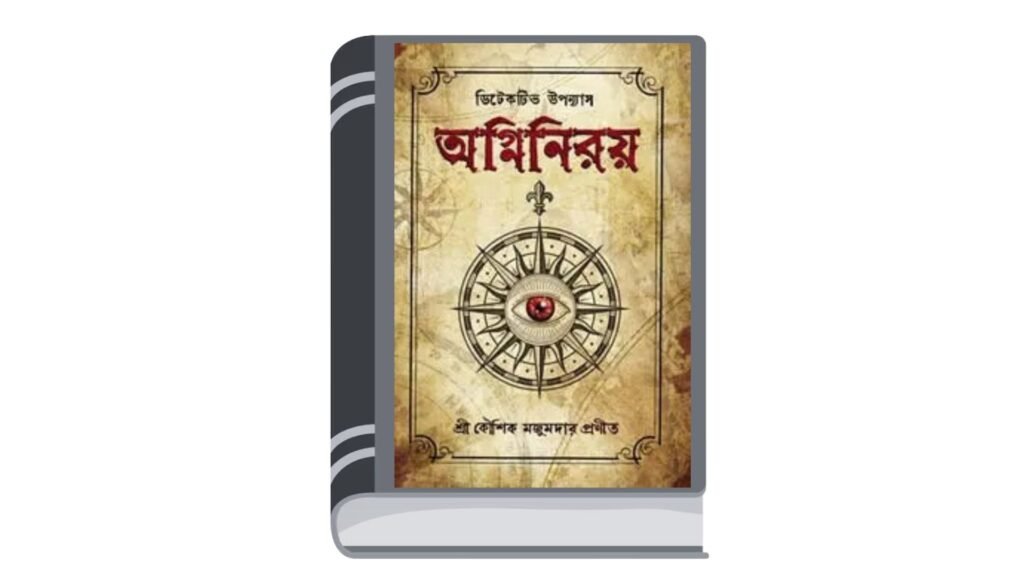লখনের কথা
১।
৪ জানুয়ারি, ১৮৯৩, চন্দননগর
কলকাতার তুলনায় চন্দননগরে ঠান্ডাটা প্রতিবার একটু বেশিই পড়ে। বিশেষ করে ভোরের দিকে। রাস্তাঘাট প্রায় নির্জন। খানিক বাদে বাদে দূর থেকে শুধু তোপের আওয়াজ শোনা যায়। এই তোপ শুনেই অনেকে ঘড়ি মেলান। ভারতের অন্য তিন ফরাসি উপনিবেশের মতো চন্দননগরও এখন পন্ডিচেরির অধীন। এক গভর্নর আছেন বটে, তবে তিনি পন্ডিচেরি ছেড়ে বিশেষ আসেন না। এখানে এক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আছেন, তিনিই সব দেখাশোনা করেন। ইদানীং এই ঘণ্টায় ঘণ্টায় তোপ দাগা, নতুন অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের পরামর্শেই করা হয়েছে।
শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সূর্যোদয়ের আগে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যেস বৃদ্ধ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের। চন্দননগরে তাঁর অবদান বড়ো কম নয়। চন্দননগর সেমিনারি স্কুল তাঁর হাতেই গড়ে উঠেছে। কিন্তু সেসব যেন কত জন্ম আগেরকার কথা। দশ বছর হল সরকারি শিক্ষাবিভাগের সর্বোচ্চ পদ স্বেচ্ছায় ছেড়ে তিনি চন্দননগরের স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছেন। লোকে জানে তাঁর শরীর ভেঙে পড়ছে। কিন্তু ভূদেব নিশ্চিত, একমাত্র উচ্চ রক্তচাপ বাদে তাঁর শরীরে কোনও সমস্যা নেই। অকালে চাকরি ছাড়ার পিছনে প্রধান কারণ দুটি- এক, সাহিত্যচর্চায় মন দেওয়া, আর দুই, যেটা প্রধান, ব্রাদারহুডের দায়িত্ব পালন।
কলকাতায় ফ্রিম্যাসনরি গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ বাহাদুরের সন্দেহের তালিকায় চলে আসেন তাঁরা। তাঁদের অগোচরেই খোচড় লাগানো হয় প্রায় প্রত্যেকের পিছনে। সামান্যতম সন্দেহ হলেই অকারণে ধরপাকড়, এমনকি সাজা দিতেও সরকার কসুর করত না। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, ইংরেজ রাজপুরুষদের অনেকেই ব্রাদারহুডের সদস্য ছিলেন। অথচ তাঁদের সাত খুন মাফ। কোপ এসে পড়ত দেশি ব্রাদারদের ঘাড়ে। মুখে যতই সবাই সমান বলা হোক না কেন, সাদা চামড়ার ইংরেজদের সমান যে এই দেশের কালা নেটিভরা কখনোই হতে পারবে না, সেটা ভূদেব বুঝেছিলেন। আর বুঝেছিলেন বলেই কলকাতার ইংরেজদের অধীনতা ছেড়ে ফরাসি চন্দননগরে এসে ঠাঁই নিয়েছেন। ফরাসি সরকারের অগোচরে তাঁদের কাজকর্ম চলে। এখানে সরকারও অবশ্য অনেক ঢিলে। তাঁদের উৎসাহ বা আগ্রহ কিছুই নেই। আর থাকবেই বা কেমন করে? তাঁদের অংশীদারি কমতে কমতে এখন মাত্র ষাট বিঘায় এসে ঠেকেছে। বাকি জমির জন্য ইংরেজরা রীতিমতো রাজস্ব নিয়ে থাকে। আর এই রাজস্ব আদায়ের জন্যেই ফরাসি সরকার দেশিমদ, গুলির আড্ডা, তুরং-এ খোলা ছাড়দিয়ে রেখেছেন। এইরকম জায়গায় ব্রাদারহুডের কাজকর্ম চালানো সহজ। ভূদেব বুদ্ধিমান। তিনি অনেক আগেই সেটা বুঝে এখানে ম্যাসনিক ব্রাদারহুডের এক গোপন সমিতি বানিয়েছেন। তাতে মূলত দেশি, অ্যাংলো আর কিছু ফরাসিদের সদস্যপদ দেওয়া হয়েছে। ইংরেজরা এর খবর জানে না।
সেদিন সকালে ভোর ছটার তোপ পড়তে না পড়তে বাড়ির চাকর এসে খবর দিল কয়েকজন নাকি তাঁকে খুঁজছে। এত সকালে? একটু অবাক হয়ে যান ভূদেব। এই সময় তাঁর স্নান আহ্নিকের সময়। এখন তিনি কারও সঙ্গে দেখা করেন না। এমনকি খুব প্রয়োজন না থাকলে ঘরের কারও সঙ্গে কথাও বলেন না। তিনি চাকরকে হাত নেড়েইশা রায় জানিয়ে দিলেন, “পরে আসতে বল।” চাকর চলে যেতে গিয়েও কী যেন ভেবে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।
ভূদেব বিরক্ত হলেন। এবার আর চুপ করে থাকা গেল না। একটু রেগেই বললেন, “যেতে বললাম তো! দাঁড়িয়ে আছিস কেন?” চাকর একটু আমতা আমতা করে বললে, “আজ্ঞে তিনজন এয়েচেন। এক কালোপানা ভদ্দরনোক। সঙ্গে এক মেয়েছেলে আর এক দুধের শিশু। দেকে মনে হল মেমসায়েবের বাচ্চা। আমি অনেক করে বললুম, বাবু একন দেকা করবেননি। তা শুনলে না। বললে নাকি খুব দরকার। একনদেকা না হলে অনথ্থ হবে।”
ভূদেবের ভুরু কুঞ্চিত হল। এত সকালে মেয়েমানুষটিই বা কে? সঙ্গে আবার শিশু কেন?
“ওঁদের বৈঠকখানায় বসিয়ে রাখ। আমি আসছি।” বলে বাসি ধুতি, কাপড়ছেড়ে নতুন কোরা ধুতি পরলেন ভূদেব। মাইকেল মধুসূদনের এই সহপাঠী হিন্দু কলেজে পড়াকালীনই কিছু বাবুয়ানি আয়ত্ত করেছিলেন। এই আটষট্টি বছর বয়সেও সেইসব অভ্যেস তাঁকে ছেড়ে যায়নি।
বসার ঘরে ঢুকে একটু চমকে গেলেন ভূদেব। সাহেবি পোশাক পরে কালো যে যুবকটি বসে আছে, তাকে কোথাও দেখেছেন। কোথায়, তা কিছুতেই মনে করতে পারলেন না। তার এক হাতের আঙুলের ডগাটা নেই। সঙ্গে স্নান মুখের সুন্দরী এক তন্বী। তার পরনেও বিলিতি পোশাক। মেয়েটির ঠিক পাশে কৌচে অপরূপা একটি চার-পাঁচ বছরের ইউরোপীয় শিশু বসে আছে। শিশুটির পোশাক মলিন। কিন্তু লাল চুল আর নীল চোখে অদ্ভুত আভিজাত্যের ছাপ। এমন দেবশিশু যেন ভূদেবের এই জমকালো বৈঠকখানাতেও বেমানান। ভূদেবকে ঘরে ঢুকতে দেখে দুজনেই উঠে হাতজোড় করে প্রণাম করল। শিশুটি একটি কাপড়ের পুতুল নিয়ে খেলছিল। সে গ্রাহ্য করল না।
ভূদেব হাতের ইশারায় তাদের বসতে বললেন। প্রথম কথা বলল ছেলেটিই, “আমার নাম ল্যানসন। লখন। আর এই আমার দিদি মারিয়ানা। আর ওর মেয়ে জিনা। বড়ো বিপদে পড়ে আমরা আপনার সাহায্যের জন্যে এসেছি।”
“বিপদ? কী বিপদ?”
“কলকাতায় ইংরেজ সরকার আমাদের খুঁজছে। আমরা কোনওমতে পালিয়ে আপনার কাছে এসেছি।”
“আমার কাছে? কে তোমাদের আমার কাছে পাঠাল? আর তোমরা কী এমন করেছ যাতে সরকার তোমাদের খুঁজছে?”
“একে একে বলি। আমি কলকাতার ব্রাদারহুডের সদস্য। সেখানে আজও আপনার কথা বলা হয়। কীভাবে ব্রাদারহুডের বিপদের দিনে আপনি……”
“থাক সেসব কথা। আসল কথায় এসো। এতদিন বাদে এই বুড়োর কাছে কেন? সমস্যায় পড়েছ যখন, সরাসরি মাস্টার ম্যাসনের কাছে যাওয়াই তোমার উপযুক্ত ছিল।”
“কলকাতার মাস্টার ম্যাসন এই মুহূর্তে আমাদের সাহায্যে অপারগ। আপনি হয়তো পত্রিকায় ইতোমধ্যে খবরটা পেয়েছেন।”
“কোন খবর?”
“করিম্বিয়ান থিয়েটারে দুই জাদুকরের মৃত্যু।”
“হ্যাঁ, তা দেখেছিলাম বটে। কিন্তু তার সঙ্গে ব্রাদারহুডের কী সম্পর্ক?”
“দুটো খুনের একটা, রিচার্ড হ্যালিডে ওরফে চিন সু লিনের খুনটা আমি করেছিলাম। মাস্টার ম্যাসনের নির্দেশে।” ভূদেবের চোখ বড়ো বড়ো হয়ে যায়। তাও তিনি বিস্ময় চেপে জিজ্ঞেস করেন,”আর অন্যটা?”
“চিফ ম্যাজিস্ট্রেট টমসন সাহেব নিজে।”
“গোটা ব্যাপারটা খুলে বলো। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।”
“আমিও গোটাটা জানি না। জানেন শুধু মাস্টার ম্যাসন। আমি যতটুকু জানি, তা বলছি। বিলাতে ফ্রিম্যাসনদের মধ্যে আমাদের একটি শাখা অনেকদিন পর আবার জেগে উঠেছে।”
“তোমাদর শাখা মানে জাবুলনরা। তাই তো?”
“হ্যাঁ। জানি আমাদের সব কাজকর্ম ম্যাসনিক ব্রাদাররা পছন্দ করেন না, তবুও ভিতরে ভিতরে অনেকেই আমাদের পক্ষে আছেন। যেমন আপনি।”
“আমি বুড়ো হয়েছি বাবা। আর বছরখানেক টিকব কি না সন্দেহ। আমাকে আর এই পক্ষে বিপক্ষে টেনো না।
“আচ্ছা। বেশ। লন্ডনের বেডলাম হাসপাতালের ডাক্তার এলি হেনকি জুনিয়ার কিছু বছর আগে অদ্ভুত একটা আরক বানান, যেটা খেলে সাময়িকভাবে একটা গোটা মানুষ বদলে যায়।”
“মানুষ বদলে যায়! বলো কী? কীভাবে?”
“চেহারায় খুব বেশি বদলায় না। বদলায় স্বভাবে। যে শান্ত, সে হিংস্র হয়ে ওঠে। যে সৎ, সে নির্বিচারে জঘন্যতম পাপ কাজ করে ফেলে। এক কথায় মানুষের চরিত্রের সবচেয়ে অন্ধকার, খল, কপট দিকটা বার করে আনে এই আরক।”
“এ কি রূপকথার গল্প নাকি হে? বিলেতে স্টিভেনসন নামে এক সাহেব এক গল্পকথা লিখেছিলেন। এ যে দেখছি অনেকটা সেইরকম। এও কি সম্ভব?”
“আজ্ঞে না হলে বলছি কেন? ধরে নিন সেই গল্প আসলে গল্প না, সত্যি কথা। সত্যিটাকে চাপা দিতে গল্পের মোড়কে মোড়ানো। মানুষের মনকে বশ করার অদ্ভুত ক্ষমতা এই আরকের। দৈহিক পরিবর্তনের মধ্যে একটাই শুধু চোখে পড়েছে। এই ওষুধের প্রভাবে থাকাকালীন নাকি হাতের চামড়া খসখসে হয়ে যায়, তালু দিয়ে ঘাম ঝরতে থাকে।”
“প্রভাব থাকে কতক্ষণ?”
“আজ্ঞে সেটা আরকের পরিমাণের উপরে নির্ভর করে। তবে এর প্রভাব ক্ষণকালের। প্রভাব শেষ হয়ে গেলে প্রভাবিত মানুষের মাঝের সময়ের কথা কিছুই মনে থাকে না।”
“ভালো কথা। আজগুবি মনে হলেও আগ্রহ জন্মাচ্ছে। বলতে থাকো।”
“বেডলামের এক কর্মচারী, নাম হিলি, সে এই ওষুধের বাক্স নিয়ে এ দেশে পালিয়ে আসে। প্রথমে কিছুদিন খোঁজাখুঁজি চলে, তারপর খবর পেয়ে বেডলামের ডাক্তার হ্যালিডেও কার্টারের ম্যাজিক শো-তে চিনা জাদুকরের ছদ্মবেশে তার পিছু ধাওয়া করে ইন্ডিয়াতে আসেন।”
“দাঁড়াও দাঁড়াও। ব্যাপারটা একটু বুঝে নিই। ছদ্মবেশে কেন?”
“আপনি তো জানেন, মহারানি ব্রাদারহুডের কাজকর্ম একটু সন্দেহের চোখেই দেখেন। বেডলামেও তাঁর চর ঘুরে বেড়ায়। তাই লুকিয়ে ছাড়া উপায় নেই। যদিও ইংরেজ গুপ্তচর বিভাগ কীভাবে যেন খবর পেয়ে এক গোয়েন্দাকে কার্টারের দলে গুঁজে দিয়েছিল।”
“কিন্তু আরকের খোঁজে সাত সমুদ্র পেরিয়ে ইন্ডিয়া আসতে গেল কেন? সেই ডাক্তার, এলি হেনকি না কী যেন বললে, সে চাইলেই তো যত ইচ্ছে আরক বানিয়ে দিতে পারত?”
“সেখানেও সমস্যা। সম্প্রতি সেই ডাক্তারের স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে। আরক বিষয়ে সব কথা তিনি ভুলে গেছেন।”
“কী মুশকিল! আরকের কোনও লিখিত ফর্মুলা তো আছে, নাকি?”
“সেটাও আমরা জানি না। হেনকির স্মৃতিভ্রংশ হবার পর তাঁর সব গবেষণার কাগজ, বই, নোটস হ্যালিডের হাতে আসে। কোথাও নাকি আরক বিষয়ে এক লাইনও লেখা নেই।”
“বলো কী হে! এমন অদ্ভুত আরক… তার ফর্মুলা নেই?”
“নেই বলেই হ্যালিডেকে ছুটে আসতে হয়েছে। যার তার হাতে এই আরক এলে কী ভয়ানক ক্ষতি হতে পারে ভেবে দেখেছেন?”
গম্ভীর মুখে মাথা নাড়লেন ভূদেব। “তা তো বটেই। মানুষের মনের উপরে স্বয়ং ঈশ্বরের দখল নেই। আছে শুধু…”
“শয়তানের”, বাক্য শেষ করে বলল লখন। “তাহলেই বুঝছেন, এই আরক হাতে পাওয়া মানে শয়তানের সমান ক্ষমতা লাভ করা। হিলি এত কিছু জানত না। সে শুধু বুঝেছিল এই বাক্স মহামূল্যবান। হিলি এ দেশে ফিরে প্রথমেই বেডলামের প্রাক্তন ডাক্তার উইলিয়াম পামারের সঙ্গে দেখা করে। হেনকির আগে পামার-ই মনোবিদ্যা বিভাগের প্রধান ছিলেন। সেখান থেকে চেনা।”
“পামার? তিনি তো শেষ বয়েসে এখানেই, মানে গোন্দলপাড়ার দিকে থাকতেন। এই তো, গত বছর মারা গেলেন। আমার সঙ্গে ভালো আলাপ ছিল। উনিও?”
“উনি ব্রাদার ছিলেন না। কিন্তু জাবুলনদের কাজকর্ম জানতেন। চাপা সমর্থনও ছিল। উনিই হিলিকে ভুলিয়েভালিয়ে কিছু টাকা দিয়ে ওষুধের বাক্সটা হাত করেন।”
“বাক্সের কথা এ দেশের ব্রাদারহুডের কানে গেল কীভাবে?”
“হিলি সুবিধের লোক ছিল না। বিভিন্ন কুকর্ম করে হরিণবাড়ি জেলে গিয়ে ঢোকে। সেখানেই তার সঙ্গে আলাপ হয় জেকব ওয়ার্নারের। আপনি চিনবেন।”
“হাড়েহাড়ে চিনি। ধরা না পড়লে কালে কালে মাস্টার ম্যাসন হতে পারত।”
“হিলি জেলে থাকাকালীন এই আরকের কথা ওয়ার্নারকে জানায়। দুজনে ঠিক করে জেল থেকে পালিয়ে আবার এই বাক্স হাতাবে। হিলি বোঝে বড্ড কমে রফা হয়েছে। কিন্তু ভাগ্য খারাপ। পুলিশ তাদের তাড়া করে। ওয়ার্নারকে ধরা গেলেও হিলি ধরা পড়েনি।”
“ধরা পড়েনি? কিন্তু আমি তো জানতাম…”
“ভুল জানতেন। হিলিরমতো একজনকে আদালতে দাঁড় করানো হয়েছিল। আসল হিলিকে কেউ বা কারা সরিয়ে দিয়েছিল। কারা কীভাবে এটা করল, সেটা আমাদেরও জানা নেই।”
“ফলে?”
“ফলে আর কী? খুবসম্ভব হিলির থেকেই ব্রিটিশ গুপ্তচরবিভাগের কাছে খবর পৌঁছে গেল। হ্যালিডে যখন আরকের খোঁজে এই দেশে এল, তখন বড়োলাট অদ্ভুত একটা শর্ত দিলেন তাকে। তিনি এই আরক খুঁজে বার করতে সাহায্য করবেন, বদলে তাঁরও একটা উপকার করতে হবে। তাঁর এক পাগল ভাই আছে। পল। যে ওষুধে স্বাভাবিক মানুষ অস্বাভাবিক হতে পারে, তাতে পাগল আবার সুস্থও হয়ে যেতে পারে। হ্যালিডে রাজি হয়নি। কিন্তু হাজার হোক বড়োলাট, তাঁকে চটিয়ে কাজ হাসিল করা মুশকিল। অন্যদিকে তিনি আর পল দুজনেই কলকাতার ম্যাসনরির সদস্য। মাস্টার ম্যাসন নিজে হ্যালিডেকে অনুরোধ করেন বড়োলাটের কথা মেনে নিতে। নিমরাজি হয়ে মেনেও হ্যালিডে কিছু শর্ত দেয়।”
“কী শর্ত?”
“বেডলামে চব্বিশ ঘণ্টা চরের নজরদারিতে এই আরক নিয়ে পরীক্ষা- নিরীক্ষা সম্ভব না। এদেশে সেই সমস্যা নেই। হ্যালিডে জানায় খাঁটি বিজ্ঞানীর মতো কিছুদিন সে অন্য পশুর উপরে পরীক্ষা চালাবে। সফল হলে সত্যিকারের কিছু পাগলের উপরে। যদি দুটোতেই সাফল্য আসে, তবেই সে বড়োলাটের ভাইয়ের উপরে আরক প্রয়োগ করবে।”
“সফল হয়েছিল?”
মাথা নাড়ল ল্যানসন। “নাহ।এই আরক একমুখী।এতে মানুষের খারাপ দিকটাই প্রকট হয়। উলটোটা হয়না। পামার মারা যাবার আগে তাঁর সমস্ত জিনিসপত্র তিনি কলকাতার ম্যাসন হলে দান করে যান। যারমধ্যে সেই বাক্সটাও ছিল। হ্যালিডেকে বাক্সটা দেখাতেই সে বোঝে, এরখোঁজেই তার এদেশে আসা। আগে এটা কেউ খুলে দেখেনি। সত্যি বলতে দেখতে পারেনি।”
“কেন?”
“এ এক অদ্ভুত বাক্স।এতে কোনও তালাচাবি নেই। বিশেষ একজায়গায় চাপ দিলে বাক্স আপনি খোলে। আর খুললেই সেখান থেকে ভূত বেরিয়ে আসে।”
“ভূত?” এবার সত্যিই চমকে গেলেন ভূদেব। “ভগবান, ভূত, শয়তান, কিছুই ছাড়ছ না যে! এরপরেও বলছ তোমার কথা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?”
অনেকক্ষণ একটানা কথা বলছিল ল্যানসন। ভূদেববাবুর চাকর এসে জল মিষ্টি দিতে গেলাস তুলে একটু জল খেয়ে আবার শুরু করল।
“আজ্ঞে, এ ভূত সে ভূতনা। বাক্সের ভিতরে চারটে বোতল আছে। অদ্ভুত চারটে লেবেল চারটে বোতলের গায়ে। B, H, U আর T। কারণ জানিনা। নম্বর হিসেবেও এদের পরপর মেশাতে হয়।”
“তুমি এতসব জানলে কীভাবে?”
মৃদু হাসল লখন, “এই যে আমার দিদিকে দেখছেন, মারিয়ানা, ওর একটা অন্য নাম আছে। ময়না। যেমন আমার লখন। এই দেশের নেটিভদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে হলে আমাদের নেটিভ নাম নিতে হয়।”
“দিদি বলছ, কিন্তু…”
“চেহারায় কোনও মিল নেই। তাই তো?” মাথা নিচু করে ল্যানসন বলল, “আমার মা কলিঙ্গবাজারে কাজ করতেন।” নিজেদের ছোটোবেলার কথা বলে গেল লখন। বলল উইলিয়াম সেটনের ময়নাকে অপহরণের কথা। কেমন করে ওয়ার্নার আর ব্রাদারহুডের সাহায্যে ময়নাকে উদ্ধার করল তার আখ্যান। ক্লাইভ স্ট্রিটের গোয়েন্দা ড্রিসকল সাহেবও অনেক সাহায্য করেছেন ময়নাকে ফিরে পেতে। তাঁর তোলা গোপন ছবি সেটনের শ্বশুরকে দেখিয়েই সেটনকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। ভূদেব মানুষটি দেখতে যতই কঠিন হোন না কেন, মন তাঁর একেবারে কোমল। তাঁর দুচোখ জলে ভরে উঠল। অজান্তেই নিজের কেদারা থেকে উঠে তিনি ময়নার মাথায় হাত রাখলেন। ময়নাও কাঁদছে। এইটুকু মেয়ে, কত কী না সইতে হয়েছে তাকে। শিশুটিও অবাক হয়ে মায়ের দিকে চেয়ে।
“আর এই মেয়ে?”
“ধরে নিন ঈশ্বরের দান।” ধরা গলায় বলে ল্যানসন।
ভূদেব বুঝলেন এঁর পিতৃপরিচয় জানতে চাওয়া মানে ময়নাকে আরও কষ্ট দেওয়া। তিনি আর কথা বাড়ালেন না। শিশুটির মুখের দিকে চেয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, “আমি বুড়ো মানুষ। আমি কেমন করে তোমাদের সাহায্য করতে পারি?”
“সেটা বলতেই এতগুলো কথা বলা। আমার বলা শেষ হয়নি। সাহেবদের পরীক্ষা করার জন্য পাগল নিয়ে আসা হত ডালান্ডা হাউস থেকে। কেউ সে আরক সহ্য করতে পারত, কেউ পারত না। মারা যেত। এ নিয়ে কাগজে বেশ হইচই শুরু হলে ডালান্ডা হাউস থেকে পাগল আনা বন্ধ হয়ে যায়। সোনাগাজির গলিতে একটা বাড়িতে এই পরীক্ষা চলত। সাহেবদের সাহায্য করত ময়না। আপনি জিজ্ঞাসা করলেন না, আমি কীভাবে সব জানলাম? ময়নাই সব জানিয়েছে। একদিন বড়োলাট নিজে জানালেন, অনেক হয়েছে, এবার সরাসরি তাঁর ভাইয়ের উপরে আরক প্রয়োগ করতে হবে। হ্যালিডে কিছুতেই রাজি হয়নি। তাকে ভয় দেখানো হয়। বলা হয়রানির এক চর তার দলে তার সঙ্গেই এসেছে, বড়োলটি জানেন। হ্যালিডে কথা না শুনলে মিথ্যে মামলায় তিনি হ্যালিডে সহ সবাইকে ফাঁসিয়ে দেবেন। তিনি বড়োলাট। তাঁর কথাই শেষ কথা। হ্যালিডে মেনে নিতে বাধ্য হয়। আর তারপরেই আসে সেই ভয়ানক সন্ধ্যা।”
“কী হয়েছিল সেদিন?”
“সোনাগাজির সেই বাড়িতে সেদিন আমাদের সবাইকে ডাকা হয়। সকালবেলাতেই গোপনে বড়োলাটের ভাই পলকে নিয়ে আসা হয়েছিল। পলকে ঘুমপাড়ানি ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হল। ঠিক হয় সন্ধের কিছু আগে
পলের ঘুম ভাঙাতে হবে। এই আরক গিলে খেতে হয়। অন্য কোনওভাবে দেহে প্রবেশ করালে কাজ হয় না। আমার এখনও মনে আছে। সেই ঘরে আমি ছিলাম, মারিয়ানা ছিল, আর ছিল পল, হ্যালিডে আর কার্টার। আর কেউ না। বড়োলাট ঢুকলেন। তবে সাধারণ ছ্যাকরাগাড়িতে। ছদ্মবেশে। পলকে জাগানো হয়েছে আধঘণ্টা হল। বড়োলাট হ্যালিডেকে নির্দেশ দিলেন আরক দিতে। সিসার লাইনিং দেওয়া বাক্সটা খুলে সব মিশিয়ে একটা সবুজ রঙের মিশ্রণ তৈরি করল হ্যালিডে। একটু জোর করেই ঢেলে দিল পলের মুখে। খানিক বাদেই পরিবর্তন দেখা দিল সারা দেহে। গোটা দেহ কাঁপছে থরথর করে। সেই শীতেও সারা গা ঘামে ভেজা। তড়াক করে উঠে দাঁড়াল সে। আমরা বসিয়ে দিতে চাইলাম। বড়োলাট চোখের ইশারায় মানা করলেন। আচমকা সবার হাত ছাড়িয়ে তিরের মতো ছিটকে বড়োলাটের টুটি টিপে ধরল পল। তার গায়ে মত্ত হাতির শক্তি। মুখ থেকে বেরোচ্ছে এক জান্তব গর্জন। আমরা তিনজন মিলে শত চেষ্টাতেও ছাড়াতে পারছি না। ময়না একপাশে দাঁড়িয়ে ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। বড়োলাট কোনওমতে কোটের পকেটে হাত ঢোকালেন। ঘরের মৃদু আলোতে আমি শুধু দেখতে পেলাম একটা ধাতব ঝলকানি। তারপরেই পলের দেহ শিথিল হয়ে গেল। ভারী বস্তার মতো এলিয়ে পড়ল মাটিতে। বুক আর পেটের সংযোগস্থলে একটা খাঁজকাটা ছুরি ঢোকানো…
.
লখন চুপ করল। ঘরের কেউ কোনও কথা বলছে না। শুধু ছোটো মেয়েটা গুনগুন করে কী যেন গান গাইছে। সুরটা বিদেশি। ভূদেব শুধু বললেন, “তার মানে আত্মরক্ষা করার জন্য…”
“তাই বলতে পারেন। কিন্তু শুরু থেকেই তাঁকে মানা করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল এ আরক মানুষের শুধু অন্ধকার দিকটা বার করে আনে। উনি শুনলেন না…”
“তারপর?”
“বড়োলাট হতভম্ব হয়ে মাটিতে বসে ছিলেন। যেন বুঝতে পারছেন না কী করা যায়। একবার শুধু মৃদুগলায় বললেন, ‘ইজ হি ডেড?’ সন্দেহের অবকাশ ছিল না। তবুও হ্যালিডে নাড়ি পরীক্ষা করে উপরে নিচে মাথা নাড়ল। ম্যাজিশিয়ান কার্টার স্তম্ভিত হয়ে গেছিল। ঘরের একপাশে হড়হড় করে বমি করে ফেলল সে। বড়োলাট তখনও স্বাভাবিক হননি। হ্যালিডেই তাঁকে বলল চলে যেতে। পলের দায়িত্ব আমরা নেব। তিনি চলে যাবার পর পলকে ফালাফালা করে চিরে ফেলা হল। অণ্ডকোশ কেটে দেওয়া হল। ওরিজেনের মতো, কিংবা যেমন করে গংসিরা খুন করে। ফেলে আসা হল চিনেপাড়ায়। ভাবা হল সব শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু সেই সন্ধে থেকেই সব কিছুর শুরু।” আবার থামল ল্যানসন।
ভূদেব অবাক হয়ে শুনছিলেন। ল্যানসন থামতেই বললেন, “এখনও বুঝলাম না, তুমি আমাকে এতসব বলছ কেন?”
“এবার আসল কথায় আসছি। যেমন প্ল্যান হয়েছিল তা ধীরে ধীরে ভেঙে পড়তে থাকে। করিন্থিয়ান হলে সাইগারসন নামের সেই সাহেব যে আসলে গোয়েন্দা, তা আমার জানা ছিল না। মাস্টার ম্যাসন পরের দিনই আমায় জানান, বড়োলাট এইসবের জন্য হ্যালিডেকে দোষী করেছেন। তাকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। আমার উপরে দায়িত্ব এল হ্যালিডেকে নিকেশ করে তার সেই বাক্স আর ফর্মুলা খুঁজে বড়োলাটকে দিতে। আমি বাক্সটা খুঁজে পাই। কিন্তু অনেক খুঁজেও ফর্মুলা পাইনি। এদিকে শুনি কার্টার ব্ল্যাকমেল করার জন্য পত্রিকা অফিসে চিঠি লিখেছিল। তাকেও খুন করা হয়েছে। তখনই আমার কেন যেন মনে হয় বড়োলাট সেই সন্ধ্যার কোনও সাক্ষী রাখবেন না। মানে একটাই। এবার আমার আর মারিয়ানার পালা। আমরা গা ঢাকা দিই। দিন কয়েক কলকাতাতেই বাগবাজারের কাছে এক গুদামে লুকিয়ে ছিলাম। কিন্তু আমার কাছে খবর আছে, ইংরেজ বাহাদুরের সেনারা আমাদের তল্লাশি চালাচ্ছে। খুঁজে পেলেই মেরে ফেলে দেবে। আর আমরা মারা গেলে দ্রিনাকেও ওরা আর বাঁচিয়ে রাখবে ভেবেছেন? হয়তো মেরে ফেলবে কিংবা কলিঙ্গবাজারে…..”
“থামো থামো! এসব আর বোলো না। তোমরা চন্দননগরে গা ঢাকা দিতে চাও। তাই তো?”
“মারিয়ানা বলল ইংরেজদের চৌদ্দ আইন থেকে বাঁচতে সোনাগাজির কিছু বেশ্যা চন্দননগরে পালিয়ে আসে। আপনি তাদের পুনর্বাসনে সাহায্য করেন। আমাদের কথা তো সব শুনলেন। এখন একমাত্র চন্দননগরেই ইংরেজ বাহাদুরের সেনারা আমাদের কিছু করতে পারবে না।”
বেশ খানিক চুপ করে বসে রইলেন ভূদেব। মাথা নিচু। শেষে বললেন, “পৃথিবীতে মানুষ যত বাড়ছে, পাপও বাড়ছে সেই হারে। তুমিও সেই পাপের অংশ। আশ্রিত না হলে তোমাকে আমি আইনের হাতে ধরিয়ে দিতাম হয়তো। কিন্তু অনেক সময় পরিস্থিতির উপরে মানুষের হাত থাকে না। তবে মানুষ নিজেকে বদলায়। বদলাতে পারে। যা হোক, আমি এক শর্তে তোমাদের আশ্রয় দিতে পারি। যতদিন আমি বেঁচে আছি ততদিন ব্রাদারহুডের কোনও কাজকর্মে যেন তোমাদের না দেখতে পাই, কিংবা কোনও অসৎ কাজে অংশগ্রহণে না দেখি। এমনকি শত প্রলোভনেও এই ভয়ানক আরক ব্যবহার করবে না। আমি বৃদ্ধ। কিন্তু সব খবরই আমার কাছে আসে। আমার কথার অবাধ্য হলে আমি নিয়ে আমাদের মিউনিসিপালিটির ফরাসি মেয়র দুমেঁ সাহেবকে বলে তোমাদের জেলে ঢোকাব। কী? রাজি? কথা দিচ্ছ?”
ল্যানসন, মারিয়ানা দুজনের চোখেই জল। তারা মাথা নেড়ে বলল, “রাজি।”
“আর সেই ভূত বাক্স?”
“সেটাও এখন আমার কাছেই আছে। মাস্টার ম্যাসন বলেছেন ওটা কলকাতায় রাখা বিপজ্জনক।”
“আগে হলে তোমার একটা কথাও বিশ্বাস করতাম না। করার মতো না। কিন্তু এখন বয়স বাড়ছে। অনেক কিছু বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে। ভগবানকে…… ভূতকে… মানুষকে। ছাড়ো সেসব কথা। আমাদের বড়বাজারের কাছেই একটা বাড়িতে তোমাদের ব্যবস্থা করে দেব। আমার বন্ধু সুরেশ বাঁডুজ্যের অনেকগুলো বাড়ি আছে। তাদেরই একটা। একটাই সমস্যা, ওকে সবকিছু খুলে বলতে হবে। তবে সমস্যা নেই। লোক ভালো। ওখানে ময়না আর তার মেয়ে থাকবে এক সাহেবের বিধবা আর তাঁর মেয়ে সেজে। তোমার পরিচয় হবে তাদের চাকরের। আপত্তি আছে?”
কোনও কথা না বলে পাশাপাশি মাথা নাড়ল দুজনে। “তবে আমার হাতে হাত রেখে দুজন মিলে একসঙ্গে শপথ নাও। আমার কী দুর্দশা হয়েছিল জানো নিশ্চয়ই?”
জীবৎকালে এই বাক্স যেন খোলা না হয়। প্যান্ডোরার বাক্স খোলার পর পৃথিবীর দুজনেই একসঙ্গে বৃদ্ধ ভূদেবের হাতে হাত রেখে শপথ নিল, “আপনি বেঁচে থাকতে আমরা কোনওরকম অসৎ কাজে লিপ্ত হব না। বাক্সও ততদিন বন্ধ থাকবে।”
তবে খুব বেশিদিন কথা রাখার দায় রইল না তাদের। পরের বছরই মে মাসে সন্ন্যাস রোগে না ফেরার দেশে চলে গেলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় ।
.
২।
ফরাসিরা চন্দননগরের অধিকার নেবার পরে বহুদিন এদেশীয়দের এড়িয়ে চলতেন। উৎসব করতেন নিজেদের মতো। ফলে দেশীয় উৎসবে শুরুতে ফরাসি ছোঁয়াচ লাগেনি। কিন্তু দিনে দিনে মেলামেশা বেড়েছে। অনেক ফরাসিরা নেটিভদের সঙ্গে সংসারও পেতেছেন। ফলে কলকাতায় বড়দিনের মতো চন্দননগরবাসীদের একান্ত নিজেদের এক পার্বণ শুরু হয়েছে। আগে এ শুধুই ফরাসিদের অনুষ্ঠান ছিল। প্রতি বছর চোদ্দোই জুলাই বাস্তিল দুর্গের পতনের স্মৃতিতে এ দেশের ফরাসিরা উৎসবে মেতে উঠতেন। তাঁদের ভাষায় এই উৎসবের নাম ফিয়েস্তা। নেটিভদের আড়ষ্ট জিভে কালে কালে তা “ফ্যাস্তা” নাম নিয়েছে। এখন গোটা চন্দননগরের মানুষ মিলে এই পার্বণে মাতেন।
উৎসবের আগের দিন থেকেই শুরু হয়ে যায় তোড়জোড়। ওই দিন পুরো স্ট্যান্ড ফরাসি পতাকা আর নীল, সাদা, লাল ফুল দিয়ে সাজানো হয়। ফরাসি সরকারি ভবনও সাজানো হয় পতাকা, ফুল, আলো দিয়ে। মেয়রের কার্যালয়ে মেয়র নিজে দাঁড়িয়ে থেকে অনাথ আর দুঃস্থদের নতুন কাপড় দান করেন। সন্ধে ছটায় হয় তোপ ধ্বনি। পরদিন সাজ সাজ রব। ঠিক ভোর ছটায় একুশ তোপধ্বনি দিয়ে মূল অনুষ্ঠানে শুরু। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে পথের দুপাশে লোকের ভিড় জমে যায়। ঝকঝকে নীল, লাল, সাদা পোশাক পরা ফরাসি পুলিশ বাহিনী কুচকাওয়াজ করে কুটির মাঠ থেকে জমায়েত হয় মেরির মাঠে 1 চারিদিকে সবাই হইচই বাধিয়ে দেয়। ফরাসি জানা অনেকে অতি উৎসাহে হেঁকে ওঠে, “লা ফেত ন্যাশিওনাল, লা ক্যাতৌযে জুইয়ে।”
এর পরেই শুরু হয় আসল মজা। ফরাসি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিংয়ের ঠিক সামনে কুড়ি ফুট উঁচু এক মাস্তুল পুঁতে, তাতে চর্বি মাখিয়ে চপচপে করে ভিজিয়ে দেওয়া হয়। চারপাশে থাকে বালি। মাস্তুলের মাথায় বিরাট একটা ঢাকা থেকে নানারকমের পুরস্কার ঝুলে থাকে। মাস্তুল বেয়ে উঠতে পারলেই মিলবে সেই পুরস্কার। প্রতিযোগীরা সেই মাস্তুল বেয়ে উঠতে চেষ্টা করে কিন্তু বারবার পিছলে পড়ে যায়। তা দেখে দর্শকরা সবাই হেসে খুন হয়। তবে সবচেয়ে মজা হয় হাঁসের খেলায়। মাঝগঙ্গায় হাঁস ছেড়ে দেন মেয়র নিজে। প্রতিযোগীরা সবাই সাঁতরে গিয়ে সেই হাঁস ধরে নিয়ে আসে। যে আগে আনবে, সেই জিতবে। এতে আবার বাজিও রাখেন অনেকে। এই খেলাটা প্রিনার খুব প্রিয়। সকাল হতে না হতে সে লখনকে তাড়া দেয় ঘাটে নিয়ে আসার জন্য। এইসব দিনে ষ্ট্যান্ডে ভয়ানক ভিড় হয়। আগেভাগে গিয়ে ভালো জায়গা দেখে না দাঁড়ালে সব মজাই মাটি।
বছর দেড়েক হল লখন চন্দননগরের বাসিন্দা হয়েছে। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ফ্যাস্তা দেখছে। এখনও এখানকার আদবকায়দার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেনি। কলকাতার চঞ্চল জীবনের পাশে কর্মহীন চন্দননগর যেন এঁদো ডোবা। কিন্তু কিচ্ছু করার নেই। যতদিন না আবার মাস্টার ম্যাসনের নির্দেশ আসে ততদিন এভাবেই তাদের থাকতে হবে। চন্দননগরে আসার পর ময়নাও কেমন যেন ঘরকুনো হয়ে গেছে। বেশিরভাগ সময় মেয়েকে নিয়েই সময় কাটে তার। দ্রিনাকে মেরির মাঠের পাশেই এক ফরাসি শিক্ষিকার ইস্কুলে ভরতি করিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফরাসির সঙ্গে সঙ্গে মেমসাহেব কাজ চালানোর মতো ইংরাজিও শেখায়।
স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে লখন আনমনে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে ছিল। আজ তার মন বড়ো চঞ্চল। এদিকে হাঁসের খেলা শেষ। এবার জনা দশেক লোক ধরাধরি করে আর-একটা চর্বি মাখানো মাস্তুল নিয়ে এসে ঘাট থেকে গঙ্গার উপরে আড়াআড়ি রেখে দিল। মাস্তুলের ডগায় ফরাসি পতাকা পতপত করে উড়ছে। যে মাস্তুলের শেষ প্রাপ্ত পর্যন্ত পৌঁছে পতাকা ছুঁতে পারবে সে-ই জিতবে। আর তার আগে হড়কে গেলেই সোজা গঙ্গায়। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে সারা বিকেল কুঠির মাঠে চলল বাচ্চাদের কানামাছি, ডিম রেস আর বস্তা দৌড়। সন্ধেবেলা সাতটার সময় আবার তোপধ্বনি হল। এই তোপ মানে এইবারের মতো উৎসবের সমাপ্তি। কিন্তু লখন জানে এত তাড়াতাড়ি দ্রিনাকে নিয়ে বাড়ি যাওয়া যাবে না। একটু পরেই শুরু হবে বাজি পোড়ানো। বাজি তৈরির কারিগররা দু-তিন মাস আগে থেকে চন্দননগরে চলে এসে বাজি তৈরি করেছে। ময়না এমনিতে ঘর থেকে বিশেষ বেরোয় না। তবে এই বাজি পোড়ানো দেখতে সেও জোড়াঘাটের চাঁদনিতে এসে হাজির। ওই জায়গাটা আবার কেবল মহিলা আর বাচ্চাদের জন্য সংরক্ষিত। দ্রিনাকে ময়নার কাছে রেখে সোজা কুঠির মাঠের দিকে পা বাড়াল লখন। আপাতদৃষ্টিতে সব স্বাভাবিক মনে হলেও সে জানে কিছু একটা গণ্ডগোল আছে। লোকটা কিছু বুঝতে পেরে ভেগেছে হয়তো।
লোকটাকে প্রথমবার লখন দেখেছিল তাদের বাড়ির উলটো দিকে। পরনে ধুতি আর ফতুয়া। রোগাভোগা চেহারা। একদৃষ্টিতে তাদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে ছিল। প্রথমে লখন গা করেনি। বাড়ির সামনে ছোটো একটা ফুলের বাগান বানিয়েছে। সেটার জন্যেই মাটি কোপাচ্ছিল সে। আড়চোখে যে সেও লোকটাকে দেখছে, সেটা বোধহয় সে বোঝেনি। দ্বিতীয় দিন আবার লখন লোকটাকে দেখতে পেল মেরির মাঠের পাশে। দ্রিনাকে হপ্তায় তিনদিন সেই ফরাসি মেমের কাছে দিতে যায়। ভূদেব মুখুজ্জে মহাপ্রাণ। এই চন্দননগরের ব্রাদারহুডের সঙ্গে কথা বলে তিনি ওদের একটা সামান্য ভাতার ব্যবস্থা করেছেন, নইলে পেটের দায়ে লখনদের আবার কাজে নামতে হত। দ্রিনার এই পড়াশুনোও সম্ভব হত না। দ্রিনাকে মেমের কাছে দিয়ে ফিরতে গিয়ে এক মোটা জারুল গাছের আড়ালে আবার লোকটাকে দেখতে পেল লখন। ইংরেজ পুলিশের খোচড় নয় তো? খুনের কেস তামাদি হয় না। লখনের খোঁজ করতে করতেই এখানে হাজির হল কি না। কে জানে? লখন দ্রুত পা চালাল। অবাক হয়ে দেখল লোকটাও তার পিছু নিল। নিজের উদ্বেগ বুঝতে না দিয়ে, হাঁটার গতি একটুও না কমিয়ে পরপর দুটো গলি পার হল সে। এবার সে নিশ্চিত লোকটা তার পিছুধাওয়া করেছে। তৃতীয় গলিটায় ঢুকেই একটা বাড়ির উঁচু রোয়াক। চট করে তার নিচে লুকিয়ে পড়ল লখন। বেশ খানিক লুকিয়ে থেকে আবার যখন মাথা তুলল, গলিতে আর কেউ নেই। ইচ্ছে করেই এদিক ওদিক ঘুরে বাড়ি ফিরল সেদিন। দ্রিনাকেও নিয়ে এল অন্য রাস্তা দিয়ে। লোকটা নেই, তবে কিছুই বলা যায় না।
মাঝে দিন তিনেক লোকটাকে আর দেখতে পায়নি লখন। ভেবেছিল আপদ গেছে। আজ ফ্যাস্তার দিনে স্ট্যান্ডে ওই ভিড়ের মধ্যে একপলকে লোকটাকে দেখেই সে আবার চিন্তায় পড়ল। শুধু চিন্তা না। ভয়। সে একা হলে সমস্যা ছিল না। ভয় ময়না আর দ্রিনাকে নিয়ে। তার কিছু হলে ওদের কী হবে? বিকেলে কুঠির মাঠে বাচ্চাদের কানামাছি খেলার সময়ও লোকটা এক কোণে দাঁড়িয়ে তাদের দেখছিল। লখনের সঙ্গে চোখে চোখ পড়তেই মাঠের উলটো দিক থেকে এগিয়ে আসতে লাগল। ভাগ্য ভালো, মাঝে একগাদা বাচ্চা দৌড়াদৌড়ি করছিল। লখন অবধি আসার আগেই সে দ্রিনার হাত ধরে আবার উলটো দিকে পা বাড়িয়ে একটা দোকানের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। মুশকিল হল, এই লখনের ভিতরে একটা ল্যানসন লুকিয়ে আছে। যে ল্যানসন মাস্টারের এক নির্দেশে খুন করতে পিছপা হয় না, ভয়ে পেয়ে পিছু হটতে জানে না, সে এমন পালিয়ে বেড়াচ্ছে ভেবে নিজেকেই মনে মনে গাল দেয় লখন। ঠিক করে আজকেই এর ফয়সালা করতে হবে। জানতেই হবে কে এই লোকটা?
সন্ধ্যায় তোপ দাগা শেষ হলে দ্রিনাকে মানার কাছে দিয়ে এবার সে উলটো লোকটার খোঁজে বার হল। ঠিকই ধরেছে। লোকটা তাকে খুঁজে না পেয়ে অবশেষে কুঠির মাঠের দিকে পা বাড়িয়েছে। এইদিন সন্ধ্যায় কুঠির মাঠে ফরাসি আর অ্যাংলো মহিলারা মেলা দিয়ে বসেন। গ্যাসের আলো জ্বেলে নানা পসরা বিক্রি হয় ছোটো ছোটো সব দোকানে। ঘর সাজানোর দারুণ সব জিনিস আর বুফ বাগিনিয়ঁ, কাসুলে কিংবা ডুফাঁনুয়াস পটেটোস-এর মতো খাঁটি ফরাসি খাবারের লোভে নেটিভরাও সেখানে জটলা পাকায়। তবে এই রাস্তা এখন ফাঁকা। ভিড় জমবে একটু পরে। বাজির খেলা শেষ হলে। লোকটা একমনে কী একটা দিশি সুর গাইতে গাইতে চলেছে। কোনও দিকে খেয়াল নেই। লখন শ্বাপদের মতো ক্ষিপ্র পায়ে লোকটার পিছুনিল। লখনের পরনেও দেশি পোশাক। ফতুয়া আর খাটো ধুতি। নেটিভ চাকরদের যেমন হয়। দ্রুত ধুতির গেঁজে খুলে ক্ষুরটা হাতে নিয়ে নিল সে। এটা সর্বদা কাছে রাখে। কী দরকারে লাগে। লোকটা গুনগুন ছেড়ে এবার খোলা গলায় গান ধরেছে। এ গান যাত্রা থিয়েটারে শুনেছে বলে মনে হল লখনের। একটু খেয়াল করে শুনল লোকটা গাইছে-
জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ
পরান সঁপিবে বিধবা বালা।
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা।
এ তো জ্যোতি ঠাকুরের নাটক সরোজিনীর গান! জ্যোতি ঠাকুর নিজেও ব্রাদারহুডে ছিলেন কিছুকাল। লখন তাঁকে চেনে। এবার গানের সঙ্গে সঙ্গে হাতে চাপড় মেরে তালও দেওয়া শুরু করল লোকটা। মানতেই হবে, গানের গলাটা খাসা। কিন্তু এ লোক লখনকে ধাওয়া করছে কেন?
কুঠির মাঠ আসার আগেই এক অন্ধকার কোণে বাঘের মতো লোকটার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল লখন। তার হাতের ক্ষুর লোকটার গলায় হালকা আঁচড় বসিয়েছে। একটু এদিক ওদিক হলেই কণ্ঠনালী দুই ফাঁক হয়ে যাবে। লোকটা এত ভয় পেয়েছিল, তার গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছিল না।
সাপের মতোফিসফিসিয়েলখন জিজ্ঞাসা করল, “তুই কে?”
লোকটা দুবার খাবি খেল। কিছু বলতে পারল না। লখন বুঝতে পারল এক আকস্মিক আক্রমণে লোকটার সারা শরীর কাঁপছে।
ক্ষুরটা একটু আলগা করে আবার একই প্রশ্ন করল।
অতিকষ্টে ধরা গলায় উত্তর এল, “ব্রাদার”
“ব্রাদার? ম্যাসন?
“নাহ। জাবুলন।”
লোকটার চেহারা, গলা সবেতেই অদ্ভুত এক কোমল, মেয়েলি ভাব। এমন লোককে ভয় পেয়েছিল ভেবে লখনের নিজেরই হাসি পায়।
“আমাকে যাওয়া করেছিস কেন?”
“ধাওয়া তো করিনি। একটা খপর দেওয়ার ছিল।”
“খবর? কী খবর?”
“আগের বড়োলাট দেশে ফিরে গেছেন। আর আসবেন না। নতুন
লাটসাহেব এয়েচেন। লর্ড এলগিন। আমাদের নোক। মাস্টার ম্যাসন আপনাকে কলকেতায় দেকা করতে বলেচেন।”
“কলকাতার কোথায়? লজে?”
“না। আস্তানায়। খুব প্রয়োজন। এটা জানাতেই আমি আপনাকে হন্যে হয়ে খুঁজে যাচ্ছি এতদিন ধরে। আর আপনি কিনা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন!”
“আমার সন্ধান কে দিল?” কঠিন গলায় শুধাল লখন।
“কে আর দেবে? মাস্টার জানতেন আপনারা চন্দননগরে আচেন। তিনি আপনাদের বন্ননা দিয়ে আমায় বললেন, তুমি ওকানের নোক। ভালো সন্ধান কত্তে পারবে। যাও, খুঁজে নিয়ে বলে এসো। আমিই খুঁজে খুঁজে… বাড়িতে আপনাকে কাজ করতে দেকে চাকর ভেবেছিলুম। আর এসব কথা নিশ্চিত না হয়ে তো বলা যায় না…. এই কাগজটাও তিনি দিয়েচেন আপনাকে দেবার জন্যে”, বলে ফতুয়ার পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ বার করে দিল লোকটা। ছাপা চিঠি। উপরেই লেখা “ইগনোর করিবেন না’। তলায় ম্যাসনদের চিহ্ন। তিনটে লোক হাতে হাতে ধরে ত্রিভুজ বানিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চিঠির মাথায় এই চিহ্নের একটাই মানে, এ চিঠি স্বয়ং মাস্টার ম্যাসন লিখছেন অন্য কোনও ব্রাদারকে। লখনের যতটুকু সন্দেহ ছিল এই চিঠি পেয়ে দূর হয়ে গেল। চিঠির ভাষা অতি জটিল, একেবারে পোড়খাওয়া লোক ছাড়া কেউ বুঝবে না। প্রাপকের নাম কোথাও নেই। প্রেরকের জায়গায় শুধু এক তর্জনী। স্বাভাবিক। ভুলবশত কারও হাতে এই চিঠি পড়লেও যেন কোনও অনর্থ না হয়। একমাত্র প্রাপক এর অর্থ বুঝতে পারবে। টকটকে লাল কালি দিয়ে চিঠিতে লেখা-
ইগনোর করিবেন না
বিনয় পূর্ব্বক নমস্কার নিবেদনঞ্চাগে মহাশয়ের রাজলক্ষী শ্রীশ্রী বিরাজ করিতরছেন তাহাতে অত্রানন্দ হয় বিশেষঃ। পরে পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ তোমার মঙ্গল শ্রীশ্রী স্থানে প্রার্থনা করিতেছি তাহাতে মঙ্গল বিশেষঃ। বহু দিবসাবধি সম্বাদ না পাইয়া বড় ভাবিত আছি মঙ্গলাদি লিখিবেন ইতি
ইগনোর করিবেন না।
চিঠি পড়ে খানিক কী যেন ভাবল লখন। তারপর বলল, “লিখিত উত্তর আর দিলাম না। আজ তো শনিবার, মাস্টারকে জানিয়ো আগামী বুধবার আমি যাব আস্তানায়। আর হ্যাঁ, পরে কোনও দিন আমার বাড়ির আশেপাশে তোমায় যেন না দেখি।”
“দেকবেন না। আমি কালই কলকাতা ফিরে যাচ্ছি। রিয়ার্সাল আছে। থ্যাটাকের। এবার তো ছাড়বেন? নাকি মেরেই শাস্তি হবে আপনার?”
গলা থেকে ক্ষুর সরিয়ে নিল লখন। থিয়েটার করে লোকটা। এত ভালো গানের গলার কারণ অবশেষে বোঝা গেল। একটু নরম সুরেই লখন বলল, নাম যেন বললে তোমার? ভুলে গেছি।”
“ভুলবেন কী করে? নাম একনও বলিনি তো! অধমের নাম শ্রীযুক্ত শৈলচরণ সান্যাল। আদি নিবাস চুঁচড়ো।”
.
৩।
সরু রাস্তা, সাপের মতো এঁকেবেঁকে দুইদিকের বাড়ির মাঝখান দিয়ে চলে গেছে। প্রায় সব বাড়ির দরজার উপরেই দুর্বোধ্য ভাষায় কী সব যেন লেখা। প্ৰায় প্ৰতি পদেই রাস্তার ধারে এক-একটা করে সরাই। সামনে ক্রেতাকে প্রলোভন দেখানোর জন্যেই হয়তো কয়েকটা ছাল ছাড়ানো, মশলা মাখানো কাঁচা মুরগি ঝুলছে। গোটা রাস্তা জুড়ে এক অজানা গন্ধ। তীব্র। বিভিন্ন মশলাপাতি মিশালে এমন ঝাঁঝালো গন্ধ পাওয়া যায়। কারও চোখ বেঁধে এই রাস্তায় ছেড়ে দিলে শুধু গন্ধেই মালুম পড়বে সে কোথায় এসেছে। চিনা ধর্মমন্দিরটার দরজা আজকে খোলা। ভিতরে তারের বাদ্য বাজিয়ে কে যেন হেঁড়ে গলায় গান গাইছে। এই সবই লখনের এককালের কত চেনা! কিন্তু এই কদিনের ব্যবধানে মনে হচ্ছে যেন কত যুগ পেরিয়ে গেছে। গলির মোড়টা ঘোরার মুখে যেখানে কিছুদিন আগেও রেড়ির তেলের বাতিস্তম্ভটা ছিল, সেখানে এখন বিজলিবাতি বসেছে। অজান্তেই সেটা দেখে একটু শিউরে উঠল লখন। এখানেই তো বড়োলাটের সেই ভাইকে…. তবে তার ভাবার সময় নেই। দ্রুত পায়ে সে চলল আস্তানার দিকে। এটার কথা ব্রাদারহুডেরও সবাই জানেন না। বাইরে থেকে অন্য পাঁচটা সরাইয়ের মতোই। ঢুকেই চার-পাঁচটা শীর্ণ টেবিল। দরজার পাশে নানারকমের খাবার, বোতল আর পাত্র সাজানো। লখন ঢুকতেই হাসিমুখে এগিয়ে এলেন দোকানের মালকিন। “কাম কাম বাবু, হোয়াত দু ইউ ওয়ান্ত?”
লখন জানে এর উত্তরে কী বলতে হয়। সে চাপা গলায় বলল, “সিয়াংদি। ব্রাদার।”
মহিলার মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়ে সামান্য উদ্বেগ দেখা দিল। “ওয়েত হিয়ার”, বলে প্রায় ছুটে ঢুকে গেলেন দোকানের পিছনের পর্দা সরিয়ে। লখন অপেক্ষা করতে লাগল। পাশের টেবিলে দুজন চিনাম্যান মাঝে মাঝে মুখের সামনে বাটি তুলে দুটো কাঠি দিয়ে কী যেন খাবার তুলে তুলে খাচ্ছে, অনেকটা সিমাইয়ের মতো দেখতে, নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, আবার কথার ফাঁকে একটু অবাক হয়েই এই কুচকুচে কালো লোকটাকে দেখছে। উপরের লাল লণ্ঠনের আলোতে সব কিছুই কেমন ভৌতিক। পাঁচ মিনিট যেতে না যেতে মহিলা ফিরে এলেন। ফুটিফাটা মুখে আবার হাসি।
“কাম বাবু, কাম”, বলে লখনকে নিয়ে চললেন দোকানের পিছনের দিকে। এখানে আলোয় ভরা লম্বা একটা ঘর থেকে টাকার আওয়াজ আর মৃদু গলার শব্দ শোনা যাচ্ছে। লখন উঁকি মেরে দেখল সে ঘরে অনেক লোক। প্রায় সবাই চিনাম্যান। সবাই একত্রে জুয়া খেলছে। টেবিলে টাকাপয়সার পাহাড় জমেছে। সে ঘর পেরিয়ে একটা সিঁড়ি নেমে গেছে সোজা নিচের দিকে। মহিলা পথ দেখিয়ে নিয়ে চলছেন। বার্নিশ করা কাঠের দরজা খুলে মহিলা পাশে সরে দাঁড়ালেন। লখন ঘরে ঢুকতে ইতস্তত করছিল। ভিতর থেকে আওয়াজ ভেসে এল, “কাম ইন।” এ গলা লখন চেনে। সে ঘরে ঢুকতেই দরজা বন্ধ করে দিলেন মহিলা। ঘরে কোনও বিজলিবাতি নেই। লণ্ঠনের আলোতে চোখ ধাতস্থ হতে খানিক সময় লাগল। তারপরেই ঘরের একেবারে মাঝে চেয়ারে বসা মাস্টার ম্যাসনকে দেখতে পেল লখন। এই কয়েকদিনেই তাঁর বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেছে। প্রায় সব চুল সাদা। চোখের কোলে কালি। লখনকে দেখেই চেয়ার থেকে উঠে করমর্দন করলেন মাস্টার। ম্যাসনিক করমর্দন। এই করমর্দন মাস্টার একমাত্র খুব বিশেষ ব্রাদার বাদে কারও সঙ্গে করেন না। তবে কি লখন আবার কোনও গুরুদায়িত্ব পেতে চলেছে? উত্তেজনায় লখনের বুক ধুকপুক করতে লাগল।
.
“আয়্যাম সরি, ব্রাদার ল্যানসন।”
মাস্টারের মুখ থেকে এমন কথা শুনবে বলে আশা করেনি লখন। সে কোনও জবাব দিল না। অপেক্ষা করতে লাগল মাস্টার কী বলেন তাঁর জন্য। মাস্টার খানিক চুপ রইলেন। হয়তো তিনি লখনের মুখ থেকেই শুনতে চাইছিলেন। লখন কিছু বলছে না দেখে তিনি আবার বললেন, “আমি জানি এখন তোমাদের একেবারে অজ্ঞাতবাসে কাটাতে হচ্ছে। আমার কথামতো কাজ করার পরেও আমি তোমাকে যথাযথ নিরাপত্তা দিতে পারিনি। এ আমার অক্ষমতা।”
আবার চুপ করলেন মাস্টার। লখন নিরুত্তর।
“তবে তুমি হয়তো জানো না, সরকারের পুলিশ যাতে তোমাদের অবধি না পৌঁছাতে পারে, তার সমস্ত ব্যবস্থা আমরা করেছি। তোমাকে খুঁজে পাবার সবকটা সূত্র, সোনাগাছির লক্ষ্মীমণি থেকে দর্জিপাড়ার নবীনচন্দ্র মান্না, কেউই আর সাক্ষী দেবার জন্য উপস্থিত নেই। সাইগারসন সাহেব দেশে ফিরে গেছেন। যেটার অপেক্ষায় ছিলাম, সেই বড়োলাটও বদলে নতুন বড়োলাট এসেছেন। ইনি আমাদের লোক। আমাদের, মানে নব্য ম্যাসনদের পক্ষে। ফলে আগের আমলে যেসব ব্রাদাররা কলকাতা ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিল, আমরা তাদের ফিরিয়ে আনতে চাইছি। জোরাজুরির কিছু নেই। তবে আমরা চাই তুমি আবার এসো। অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে। তোমাকে ছাড়া সেসব কাজ হবে না।”
খানিক কী যেন ভাবল লখন। তারপর বলল, “এই প্রস্তাবে না বলার সুযোগ আছে?”
মাস্টার বোধহয় এটা আশা করেননি। তাঁর মুখ কঠিন হল। চোয়াল শক্ত। খুব ধীরে দাঁতে দাঁত চেপে তিনি বললেন, “না করার কারণ জানতে পারি কি?”
“আমি তো এখন একলা নই আর। বাকি দুইজনকে আমার জন্য বিপদে ফেলতে পারি না।”
হো হো করে হেসে উঠলেন মাস্টার ম্যাসন। হাসতে হাসতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। লখনের দুই কাঁধে হাত দিয়ে লখনের মুখের খুব কাছে নিজের মুখ নিয়ে এলেন। তাঁর মুখ থেকে এলাচের মৃদু গন্ধ ভেসে আসছে। কাটা কাটা গলায় বললেন, “যা তোমার না, যা তোমার কোনও দিন হবে না, তার দাবি করছ কেমন করে? তুমি ব্রাদারহুডের সামান্য কর্মী। মনে রাখবে। তোমার দায়িত্ব কী?”
লখন চুপ।
মাস্টার এবার তীব্র স্বরে বলেন, “তোমার দায়িত্ব কী?”
“মাস্টারের আজ্ঞা পালন”, ধীর কন্ঠে উত্তর দেয় লখন।
“যাক! ভোলোনি দেখছি! আর আজ্ঞা পালন না করলে কী হয়?”
“বিনাশ।”
“গুড। এক হপ্তা সময় দিলাম। চন্দননগরের পাট চোকাও। কলকাতায় কিড স্ট্রিটে ঘর দেখা হয়েছে। সেখানেই থাকবে তোমরা। এখন যেভাবে আছ।”
“ঠিক আছে মাস্টার।”
“আর হ্যাঁ। তোমাকে যে দুটো সম্পত্তির দায়িত্ব দিয়েছিলাম, সে দুটোর কী খবর?”
“দুটোই ঠিক আছে।”
“সময় ঘনিয়ে আসছে। ব্রাদারহুড এতদিন ঘুমিয়ে ছিল। এইবার সুযোগ এসেছে প্রত্যাঘাতের। কোনওমতেই যেন আমরা এই সুযোগ না হারাই। এমন সুযোগ একবারই আসে। ময়না কতটুকু জানে?”
“শুধু জানে মা-মরা মেয়ে। কলিঙ্গবাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ব্রাদারহুড তাকে উদ্ধার করেছে।”
“ব্যস! আর কিছু জানানোর প্রয়োজন নেই। সময় হলে সব জানবে। আর সেই বাক্স?”
“মাস্টারের আদেশ ছাড়া ওই বাক্সে হাত দিইনি।”
“খুব ভালো। তুমি কলকাতায় চলে এসো। তারপর তোমাকে নতুন কাজ দেব। হাসপাতালে।”
“আবার ডালান্ডায়?”
“না। ওখানে প্রিয়নাথ একবার তোমাকে দেখে ফেলেছিল। এখন প্রায়ই ডালান্ডায় পুলিশের খোচড় ঘুরে বেড়ায়। তোমায় কেউ চিনে নিলে মুশকিল। তুমি যাবে প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে। ডাক্তার কানিংহ্যাম বুড়ো হয়েছেন। তাঁর ল্যাবরেটরিটা আগের মতো ব্যবহার হয় না। ইদানীং তাঁর এক ছাত্র সেখানে কাজ করেন। কিছুদিন আগে অবধি ল্যাবরেটরিতে ধোয়ামোছার জন্য রামেশ্বর নামের একজন ঢুলি ছিল। গত সপ্তাহে সে মারা গেছে।”
“কীভাবে মারা গেল?” না চাইতেই লখনের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।
“তাতে তোমার কী দরকার হে? তবে জানতে চাইছ যখন বলেই দিচ্ছি, রামেশ্বর ছিল ক্যানিংহ্যামের ডান হাত। একদিন বাড়ি ফেরার পথে কিছু ডাকাত তার উপরে চড়াও হয়ে পেটে ছুরি ঢুকিয়ে মেরে ফেলে। এবার তোমাকে ওর জায়গাটা নিতে হবে। তোমার সুপারিশপত্র তৈরিই আছে। ক্যানিংহ্যামের ল্যাবরেটরিতেই আমাদের এক ব্রাদার এখন কাজ করছেন। তুমি তাঁকে সাহায্য করবে। তুমি একা না। আরও একজন মহিলা আছেন। মঙ্গলা নাম। সেও ধোয়ামোছার কাজই করে। আমাদেরই লোক।”
“ঠিক কী ধরনের সাহায্য করব আমি?”
“কিচ্ছু না। তুমি তোমার সেই ভূতের বাক্সটা এনে আমাদের ব্রাদারকে দেবে। তিনি ওটা নিয়েই গবেষণা করবেন।”
“কী গবেষণা?”
“সেটা আমাদের চেয়ে তিনিই ভালো বুঝবেন, তাই নয় কি? দাঁড়াও। তিনি পাশের ঘরেই আছেন। তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।”
ঘরের লাগোয়া যে আরও একটা দরজা দেওয়ালে প্রায় মিশে আছে, সেটা এতক্ষণ খেয়াল করেনি লখন। মাস্টার সেই ঘরের দরজা খুলে কাউকে একটা আহ্বান করলেন। ছোটোখাটো চেহারার এক নেটিভ ভদ্রলোক ঘরে উপস্থিত হলেন। লখন তাঁকে দেখে উঠে দাঁড়াল ।
“এই হল লখন। যার কথা আপনাকে বলছিলাম। আর লখন, এঁকে চিনে রাখো, এখন থেকে ইনি যা বলবেন তোমাকে সেইমতোই চলতে হবে। ইনি ক্যানিংহ্যাম ল্যাবরেটরির নতুন ডাক্তার, আগে মেডিক্যাল কলেজে ছিলেন, মহেন্দ্রলাল সরকারের ছাত্র ডাক্তার গোপালচন্দ্র দত্ত। হাটখোলার দত্ত বাড়ির ছেলে।”
.
৪।
১৭৫৮ সালের মাঝামাঝি রেভারেন্ড জন জ্যাকেরিয়াস কিয়েরেন্ডার কলকাতায় পা রাখলেন। প্রোটেস্টান্ট চার্চ থেকে তাঁকে গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, কলকাতার নেটিভদের মিশনারি শিক্ষার আলোতে আলোকিত করার। কলকাতায় এসেই কাজে নেমে পড়লেন কিয়েরেন্ডার। প্রচুর জায়গা-জমিও কিনে মিশন রো এলাকায় প্রথম প্রোটেস্টান্ট প্রেয়ার হাউস তৈরি করেন, মুখে মুখে যা ওল্ড মিশন চার্চ নামে পরিচিত হল। এরই খুব কাছে, বর্তমানের এক নম্বর গারস্টিন প্লেস- এ ছিল শুধুমাত্র সাহেবদের জন্য প্রেসিডেন্সি হসপিটাল। হাসপাতাল থাকলেও সেখানে যতজন সাহেব ঢুকতেন তাঁদের প্রায় কেউই জীবিত অবস্থায় বেরিয়ে আসতেন না। তাঁদের সরাসরি নিয়ে যাওয়া হত পাশেই ঠিক উত্তর-পশ্চিম কোণের প্রাচীন গোরস্থানে। ভারতে আসা সাহেবদের ক্রমাগত চাপে কোম্পানি নতুন হাসপাতাল তৈরির কথা ভাবল। ময়দানের উলটো দিকে জ্যাকেরিয়ার এক প্রকাণ্ড বাগানবাড়ি ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মোটা টাকায় সেই জায়গাটা তাঁর কাছ থেকে কিনে নেয়। পাশেই ছিল এক বাঙালি ভদ্রলোকের অনেকটা জমি বাড়ি। সেটাও কিনে নিল কোম্পানি। ১৭৭০ সালের এপ্রিলে শেষ হল হাসপাতাল তৈরির কাজ। নতুন এই হাসপাতালের নাম রাখা হল প্রেসিডেন্সি জেনারেল হসপিটাল। লোকের মুখে মুখে পিজি হাসপাতাল। ঠিক করা হল, শুধু চিকিৎসা না, সময় মোতাবেক আধুনিক চিকিৎসানিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা আর গবেষণাও করা হবে এখানে।
ডাক্তার ক্যানিংহ্যাম-ও সেই কাজেই লন্ডন থেকে কলকাতা এসেছিলেন। জাতে স্কটিশ এই চিরকুমার মানুষটির ধ্যানজ্ঞান ছিল গবেষণা। কলকাতায় এসে নিজের গবেষণাগারে কলেরা নিয়ে যে কটা পেপার প্রকাশ করেছিলেন, প্রত্যেকটা বিজ্ঞানের এক-একটা মাইলস্টোন। বেশ কিছুদিন মেডিক্যাল কলেজে পড়িয়ে এখন শুধু গবেষণা আর পড়াশোনা করেন। দেশবিদেশের নানা আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে সাজিয়েছেন নিজের গবেষণাগার। অবশ্য বয়স বাড়ায় নিজে আর খুব বেশি কাজ করতে পারেন না এখন। করে তাঁর ছাত্ররা। ছাত্রের সংখ্যাও অবশ্য ইদানীং কমতে কমতে একটিতে এসে ঠেকেছে। কোনও অজানা কারণে ইদানীং ক্যানিংহ্যামের গবেষণাগারে ছাত্র আসা বন্ধ হয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও তাঁকে আর ছাত্র দিচ্ছেন না। ক্যানিংহ্যাম কারণ জিজ্ঞাসা করেছেন। চিঠি দিয়েছেন। কোনও সন্তোষজনক উত্তর পাননি। সবেধন নীলমণি ছাত্রটি অবশ্য মেধাবী। মেডিক্যাল কলেজের নামী ডাক্তার। তাঁর এককালের ছাত্র। উচ্চতর গবেষণার জন্য সে খামোখা কেন মেডিক্যাল কলেজ ছেড়ে তাঁর কাছে এল, বুঝতে পারেন না ক্যানিংহ্যাম। হয়তো আধুনিক রসায়ন আর জীবাণুবিদ্যাচর্চায় তাঁর ল্যাবরেটরিটা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে সেরা বলে। লন্ডন থেকে ডাক্তার প্রিয়ার্সন যে মানব নাভতন্ত্রের আধুনিক মডেলটি পাঠিয়েছেন, সেটিও একমাত্র তাঁর কাছেই আছে। ডাক্তার টাইটলার তাঁকে দিয়েছিলেন মস্তিষ্কের আর মানবকঙ্কালের সম্পূর্ণ চিত্র। কিন্তু ছাত্রটির কাজের সঙ্গে এসবের কী সম্পর্ক? যতদূর তিনি জানেন, সে একজন সার্জন। তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে এড়িয়ে যায়। হাসে। বলে, “আপনার দেখানো পথে কাজ করতে চাই।” যদিও কতটা কী পথ দেখাতে পারছেন, সে বিষয়ে ক্যানিংহ্যাম সন্দিহান। শারীরবিদ্যার চেয়ে মনস্তত্বে ছাত্রটির আগ্রহ বেশি। দিনরাত ল্যাবরেটরিতে পড়ে থাকে। মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব প্রশ্ন করে। এই যেমন সেদিন আচমকা জিজ্ঞাসা করল, “আচ্ছা স্যার, এমন কি কোনও পদ্ধতি আছে, যাতে কোনও ওষুধ প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে কাজ করবে না। করবে ঘণ্টাখানেক বা ঘণ্টা দেড়েক বাদে?” কিংবা “কীভাবে কোনও বিক্রিয়ার সময় বাড়ানো যাবে?” এসব অবাস্তর প্রশ্ন সে কেন করে সাহেব বোঝেন না। হিসেবমতো তার কাজ মানুষের স্নায়ু ও বিভিন্ন স্নায়বিক রোগ নিয়ে। রোগের ধরন দেখাই তার কাজ। অন্তত এমনটাই বলেছিল সে। কিন্তু যা মনে হচ্ছে, ল্যাবরেটরিতে সে অন্য কিছু করে। সেদিন আচমকা ল্যাবরেটরিতে ঢুকে দেখেন তাঁর ছাত্র নানারকম দ্রবণ মিশিয়ে কী যেন বানাচ্ছে, গোটা ঘর ধোঁয়ায় ভর্তি। ক্যানিংহ্যাম যতটা চমকেছিলেন, তাঁর ছাত্রটিও কম চমকায়নি। “এসব কী হচ্ছে?” জিজ্ঞাসা করায় সে প্রথমে আমতা আমতা করে। পরে বলে, পাশেই ডালান্ডা হাউসের কিছু পাগল উন্মত্ত হয়ে তাণ্ডব চালাচ্ছে। তাদের শান্ত করে ঘুম পাড়ানোর জন্যেই নাকি পি জি হাসপাতালের ডিরেক্টর তাকে এই কাজ দিয়েছেন।
অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেন ডাক্তার ক্যানিংহ্যাম। তিনি এ দেশের নেটিভদের অপছন্দ করেন না। বরং ভালোবাসেন বলা যায়। কিন্তু এক নেটিভ তাঁরই গবেষণাগারে বসে, তাঁকেই না জানিয়ে দিনের পর দিন কাজ করে যাবে, সেই চিন্তাও তাঁর কাছে অসহ্য। আর সইতে না পেরে একদিন তিনি ডিরেক্টরের দ্বারস্থ হলেন। ডিরেক্টর সোজা জানিয়ে দিলেন কলকাতার বনেদি পরিবারের এই সস্তানের হাত অনেক দূর অবধি বিস্তৃত। সহজে কেউ তাঁকে ঘাঁটায় না। খুব উঁচু থেকে তাঁর জন্য সুপারিশ এসেছে। ডিরেক্টরের কিছু করার নেই। ক্যানিংহ্যাম- ও যেন এসবে মাথা না গলান।
বৃদ্ধ ডাক্তার নিজের কাজের জায়গাতেই ব্রাত্য হলেন। তিনজন নেটিভের মধ্যে মৌলাবক্স আর মঙ্গলা আগে থেকেই কাজ করত। এখন একজন নতুন লোক এসেছে। পোশাকে নেটিভ। কিন্তু হাবেভাবে একটা ইউরোপীয় ব্যাপার আছে। সম্ভবত হাফব্লাড। অ্যাংলো। গায়ের রং কুচকুচে কালো, কিন্তু চোখ দুটো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। সে বেশি কথা বলে না। শুধু স্থির হয়ে তাকিয়ে থাকে। সে চোখের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। ছেলেটার হাতের একটা আঙুলের ডগা নেই।
আজকাল রাত বাড়লে ল্যাবরেটরিতে আলো জ্বলে। খুটখাট কী সব কাজ হয় যেন। অচেনা মানুষদের আনাগোনা বাড়ে। একদিন ক্যানিংহ্যাম প্রায় মধ্যরাতে জলতেষ্টা পাওয়ায় উঠেছিলেন। জানলা দিয়ে ল্যাবরেটরির ঘষা কাচের শার্শি দেখা যায়। চমকে উঠে তিনি দেখলেন, এই মাঝরাতে ল্যাবরেটরিতে বেশ কিছু ছায়ামূর্তি উত্তেজিত হয়ে ঘোরাঘুরি করছে। তিনি ভাবলেন নিশ্চয়ই চোর ঢুকেছে। রাতের পোশাক পরেই ল্যাবরেটরির দিকে যেতে পথ আটকে দাঁড়াল সেই ছেলেটা। চোস্ত ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে বলল, “এত রাতে ল্যাবরেটরিতে যাবেন না স্যার। বিপদ হবে।”
“কীসের বিপদ? ল্যাবে চোর ঢুকেছে। সরো এখান থেকে”, বলে তাঁকে সরাতে যেতেই ইস্পাতকঠিন হাতে তাঁর দুই কাঁধ চেপে ধরল ছেলেটা। ক্যানিংহ্যামের সারা শরীর যেন অবশ হয়ে যেতে লাগল।
“চলুন স্যার, আপনাকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি”, বলে প্রায় ঠেলেই তাঁকে ঘরে পৌঁছে দিল সে।
নিজের হাতে গড়া ল্যাবরেটরিতে ক্যানিংহ্যামের সেই শেষবারের মতো যাওয়ার চেষ্টা। পরের দিন সকালেই তিনি দেশে ফেরার আবেদন করলেন। “বয়স হয়েছে। এবার নিজভূমে শাস্তিতে মরতে চাই।”
প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আর্জি মঞ্জুর হল। কেউ একবারের জন্যেও বলল না, থেকে যান। পরের মাসেই খিদিরপুর ডক থেকে আটলান্টা জাহাজে চেপে শেষবারের মতো চোখের জলে ভারতকে বিদায় দিলেন ডাক্তার ডেভিড ডগলাস ক্যানিংহ্যাম।
.
৫।
এমন নিস্তরঙ্গ জীবনই কি চেয়েছিল লখন? চন্দননগরে ক্রমাগত কর্মহীনতা তাকে ক্লাস্ত করে তুলেছিল। ভেবেছিল কলকাতায় নিয়ে এসে মাস্টার তাঁকে কোনও গুরুদায়িত্ব দেবেন। তিনি কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু এ কেমন কাজ? প্রায় সারাদিন নিশ্চুপ বসে থাকা ক্যানিংহ্যামের ল্যাবরেটরির সামনে। মাঝেমাঝে গোপালচন্দ্র টুকটাক সাহায্যের জন্য ডাকে। কিন্তু মূল সাহায্যকারী মঙ্গলাই। এই মঙ্গলা এক অদ্ভুত মহিলা। জাতে বাগদি, কিন্তু চেহারা ব্রাহ্মণকন্যার মতো। অকারণে কথা বলে না। মুখ বুজে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে। দুই বছর কেটে গেল। যে উত্তেজনার টানে লখন এক কথায় কলকাতায় ফিরে এসেছিল, তার কণামাত্র অবশিষ্ট নেই। একবার ঠারেঠোরে সে ব্রাদারহুডকে জানিয়েছে। মাস্টার মৃদু হেসে শুধু বলেছেন, “তৈরি থাকো লখন। ভয়ানক একটা ঝড় আসতে চলেছে। সেই ঝড়ে সব ওলটপালট হয়ে যাবে। এই থমথমে শাস্ত ভাব আসলে ঝড়ের আগের পূর্বাভাস মাত্র। যেদিন ঝড় আসবে, আমি কথা দিচ্ছি, সবার আগে জানতে পারবে তুমিই।” লখন শিকারি বাঘের মতো অপেক্ষায় বসে থাকে। ইদানীং গোপালচন্দ্র নিজে প্রায়ই কোথাও বেরিয়ে যান। ফেরেন বেশ কয়েক ঘণ্টা বাদে। হাতে ছোপ ছোপ কালি মাখা কাগজের তাড়া। আজকাল আর নানা কেমিক্যাল মিশিয়ে বকযন্ত্রে ফোটান না গোপাল। বরং আতশকাচ নিয়ে সেইসব কালিমাখা কাগজে কী যেন খুঁজতে থাকেন।
লখনের এখনও মনে আছে সেই রাতের কথা। মধ্যরাত্রি প্রায় অতিক্রান্ত। মাস্টারের কড়া নির্দেশ, গোপাল ল্যাবরেটরিতে থাকাকালীন তাঁর অনুমতি ছাড়া কাউকে ঢুকতে দেওয়া যাবে না। লখন তাই বসে আছে দরজা জুড়ে। হয়তো ঘুমে চোখ একটু ঢুলেই এসেছিল, হঠাৎ এক তীব্র চিৎকারে তার ঘোর কেটে গেল। পড়ি কি মরি করে দৌড়ে ভিতরে ঢুকে দ্যাখে এক অদ্ভুত দৃশ্য। হলদে বিজলিবাতির একটা টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে সাইডটেবিলে, আর এক হাতে আতশকাচ, অন্য হাতে একটা কাগজের ফালি নিয়ে দুই হাত উপরে তুলে গোপালচন্দ্র নাচছেন। দৃশ্যটা এতই আকস্মিক আর অভাবনীয় যে লখন প্রথমেই ভাবল ডালান্ডা হাউসের কোনও পাগল ছাড়া পেয়ে ল্যাবে ঢুকে গেছে, অথবা কাজের চাপ সইতে না পেরে গোপালচন্দ্র উন্মাদ হয়ে গেছেন। লখনকে দেখতে পেয়ে নাচ কমল তো না, বরং বাড়ল। দুই হাতে লখনকে জড়িয়ে ধরে, ভুল তালে, হেঁড়েগলায় গোপাল “পেয়েছি রে পেয়েছি” বলে প্রায় লাফাতে শুরু করলেন। প্রথমে খানিকক্ষণলখন বাধা দেয়নি, তারপর গোপালের দুই হাত ধরে “শান্ত হোন ডাক্তারবাবু, এসব কী? এসব শিশুপনা কি আপনার মতো মানুষকে মানায়?” বলতে গোপাল কিছুটা স্বাভাবিক হলেন। তখনও তাঁর দুই চোখ আনন্দে জ্বলজ্বল করছে।
“নাচছি কেন? নাচছি আনন্দে। এই দ্যাখো কী পেয়েছি”, বলে দুটো কালিমাখা কাগজ লখনের চোখের সামনে মেলে দিলেন। লখন কিছুই বুঝল না। কী এসব? কেনই বা এতে এত উত্তেজনা?
এবার গোপালও নিজে বুঝলেন কেন তাঁর আনন্দ লখনের মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে না।
“এ হে, আমারই ভুল। তোমায় কিছু না বুঝিয়ে একেবারে ফলাফল দেখাচ্ছি। কাছে এসো।”
লখন কাছে আসতেই তার হাত দুটো ধরে টেবিল ল্যাম্পেরতলায় এনে চেটো দুটো উলটে রাখলেন ডাক্তার গোপাল।
“কী দেখতে পাচ্ছ?”
“নিজের হাত”, গোপালের মাথাটা কি সত্যিই গেছে? মনে মনে ভাবল লখন।
“হাতের চেটোয় কোনও দাগ দেখতে পাচ্ছ না?”
অনেক খেয়াল করে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রচুর দাগ চোখে পড়ল লখনের। আগে কোনও দিন খেয়াল করেনি।
“এবার বাঁ হাতটা বাড়াও।”
যন্ত্রের মতো বাঁ হাত বাড়াতেই তাতে কালির একটা রোলার ঘষে দিলেন গোপাল। তারপর বললেন, “এবার এই সাদা কাগজে হাতটা চেপে ধরো।” লখন চেপে ধরল। কিন্তু কেন এসব হচ্ছে, কিছুই তার মাথায় ঢুকছে না।
“ব্যস। এবার উঠিয়ে নাও। তোমার হাতের ছাপ তৈরি।”
এবার লখন অবাক হল। এতক্ষণ হাতের যে সূক্ষ্ম দাগগুলো তার চোখেই পড়ছিল না, তারা প্রায় সবাই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে এই সাদা কাগজের বুকে। লখন এই প্রথমবার আগ্রহী হল।
লখনের চোখ মুখ দেখেই গোপাল সেটা বুঝতে পেরেছেন। এবার মৃদু হেসে বললেন, “কেমন? পুরো ম্যাজিক, তাই না? আসলে এ একেবারে আধুনিকতম বিজ্ঞান। সবে দুই-আড়াই বছর হল এ সম্পর্কে জানা গেছে। এখনও অনেক কিছু জানা বাকি। আমাদের ইনস্পেকটর জেনারেল এডওয়ার্ড রিচার্ড হেনরি আর তাঁর দুই নেটিভ সঙ্গী আজিজুল হক আর রায়বাহাদুর হেমচন্দ্র বসু এ নিয়ে নিত্যনতুন গবেষণা করছেন। আর তা থেকেই অদ্ভুত সব খবর পাওয়া যাচ্ছে।”
“যেমন?”
“যেমন? এই যে ধরো তোমার হাতের ছাপ। এই কাগজে। এই ছাপ একান্তই তোমার। একবারে নিজস্ব। এই গোটা বিশ্বে তোমার মতো দেখতে লোক অনেক থাকতে পারে, কিন্তু এই হাতের ছাপের মালিক একজনই। তুমি। এর অর্থ বুঝতে পারছ?”
মাথা নাড়ল লখন। পারছে না।
“এতদিন অনেক অপরাধী এই মর্মে ছাড়া পেয়ে যেত যে, অপরাধের সময় আমি সেখানে ছিলাম না। সাক্ষী থাকলেও বলা হত, তার মতো কাউকে দেখেছে। অনেক সময় অপরাধীর পক্ষে বেশ কিছু সাক্ষী জোগাড় হত, যারা দিব্যি গেলে বলত অপরাধের সময় আসামি অকুস্থলে ছিলই না। এবার ভাবো, যদি কোনওমতে অকুস্থলে আসামির হাতের ছাপ পাওয়া যায়, আর সেটা তার সঙ্গে মিলে যায়, তবে স্বয়ং ভগবান এসে বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না আসামি এই কাজ করেনি। কারণ একই হাতের ছাপ শুধু একজনেরই হয়।”
“কিন্তু যমজ ভাই বা বোন হলে?”
“এখানেই তো মজা। যমজদের সব এক। কিন্তু হাতের ছাপ আলাদা। ঈশ্বরের এই এক অদ্ভুত সৃষ্টি। প্রতিটা মানুষকে তিনি একেবারে নিজস্ব হাতের ছাপ দিয়ে পাঠিয়েছেন।”
এইটুকু বলে গোপাল চুপ করে কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, “ব্রাদারহুডে একটা কথা আছে জানো তো? ঈশ্বরের সৃষ্টিকে একজনই মাত্র অস্বীকার করতে পারে?”
“হ্যাঁ। জানি। শয়তান।”
গোপালচন্দ্র কিচ্ছু না বলে টেবিল ছেড়ে উঠে গেলেন। যখন ফিরে এলেন, তাঁর হাতে লখনের সেই চেনা বাক্স। দীর্ঘ প্রায় দুই বছর তাঁর কাছেই এ বাক্স ছিল। তালাচাবি নেই। একটা মাত্র বিশেষ পদ্ধতিতেই খোলা যায়।
“এই বাক্সে শয়তান পোরা আছে। স্বয়ং শয়তান। আমার সন্দেহ হচ্ছিল। আজ নিশ্চিত হলাম।” একটু আগেও নতুন কিছু খুঁজে পাওয়ার যে আনন্দ গোপালের গলায় ছিল, তা সম্পূর্ণ হারিয়ে গিয়ে অদ্ভুত এক ভয় যেন বাসা বেঁধেছে।
“আমাকে এই ল্যাবরেটরিতে কী কাজ দেওয়া হয়েছিল তুমি জানো?”
পাশাপাশি মাথা নাড়ল লখন। সে জানে না। ব্রাদারহুড়ে একজন কর্মীর এত কিছু জানার অধিকার নেই।
“কিন্তু তোমার জানা উচিত। হাজার হোক তুমি আমার সহকারী। গবেষণাগারে যতটা করা যায় আমি করেছি। এবার সরাসরি এটা প্রয়োগ করতে হবে। আর সেই কাজে তুমি ছাড়া গতি নেই। তাই কাকেই বা বলব এসব?”
লখন বুঝতে পারছিল না আলোচনাটা কোনদিকে এগোচ্ছে। কিন্তু দীর্ঘ এই ক্লান্তিকর বসে থাকার চেয়ে ভালো কিছু, এটুকু বুঝতে পারল।
“এই BHUT নিয়ে তো অনেক কিছুই জানো তুমি। একটা গোটা মানুষকে বদলে দেয়। যদিও সাময়িক। এই আরক মানুষের সবচেয়ে নিকৃষ্ট, হিংস্র দিকটাকে বাইরে বার করে আনে। এ সবই তোমার জানা। কিন্তু এই আরকের একটা সমস্যা আছে। চারটে আরক পরপর মিশিয়ে এটা তৈরি করে সঙ্গে সঙ্গে খাওয়াতে হবে, নইলে কাজ হবে না। কাজও হবে সঙ্গে সঙ্গে। এর অসুবিধা দুটো। একে তো হাতে সময় পাওয়া যায় না, তোমাকে চারটে আরকের বাক্স নিয়ে ঘুরতে হবে, আর দুই, যেটা সবচেয়ে সমস্যার, যার ওপরে তুমি এটা প্রয়োগ করবে, তার অজ্ঞাতে এটা খাইয়ে দেওয়া প্রায় অসম্ভব।
“ঠিক। এটা আমিও ভেবেছি”, বলল লখন
“আর ক্যানিংহ্যামের এই ল্যাবরেটরিতে এটাই আমার কাজ ছিল। এমন কিছু বানানো, যাতে এই আরকের কাজ খুব ধীরে ধীরে হয়, ফলে হাতে সময় থাকে আর যাকে দেওয়া হবে তার অজ্ঞাতে এই আরক খাইয়ে দেওয়া সম্ভব হয়।”
“তারপর?”
“খাঁটি বিজ্ঞানীর মতো আমি প্রথমে এলিমেন্টাল অ্যানালাইসিস করতে চাইলাম”, বলে লখনের হতবাক মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের ভুল বুঝতে পারলেন গোপালচন্দ্ৰ।
“ওহ। দুঃখিত। তোমাকে এসব বলছি কেন? সোজা কথায় এই চারটে আরকে কী কী আছে দেখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মাস্টার মানা করেন। কারণ আরকের পরিমাণ কম, আর শেষ হলে নতুন করে বানানোর ফর্মুলা আমরা কেউ জানি না। বদলে আমি অন্য একটা কাজ শুরু করি। গত দুই বছরে আমি এমন একটা বড়ি আবিষ্কার করেছি, যা জলে দিয়ে দিলে গলে যায়, আর তার ভিতরের রাসায়নিক খুব ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে কাজ করে। এবার বড়ির মধ্যে আলাদা আলাদা চারটে আরক যদি খুব অল্প পরিমাণে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তবে খাদ্য বা জলের মাধ্যমে এই মিশ্রণ মানুষের শরীরে প্রবেশ করার বেশ খানিক বাদে কাজ শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে না।”
“অভিনন্দন আপনাকে।”
“ধন্যবাদ। কিন্তু এইজন্য আমি একটু আগে পাগলের মতো নাচিনি। নেচেছি অন্য কারণে।
“কী কারণ?”
“আর-একটু জ্ঞান দিই তোমায়। এই দ্যাখো তিনরকম আঙুলের ছাপ।
প্রথমটায় দাগগুলো একদিক থেকে শুরু হয়ে, আর একদিকে শেষ হয়েছে। এদের বলে আর্চ। পাঁচ শতাংশের কম সংখ্যক মানুষের হাতের ছাপে আৰ্চ দেখা যায়। দুই নম্বরই সবচেয়ে বেশি। দাগগুলো যেদিক থেকে শুরু হয়েছে, ঘুরে এসে সেদিকেই মিলেছে। এদের নাম লুপ। আর লুপের পরেই যেটা বেশি দেখা যায়, তা হল তৃতীয়। ঘূর্ণিপাকের মতো নকশা। একে বলে হোর্ল। এদেরই বিভিন্নরকম এদিক ওদিক করে হাতের ছাপ নির্ণয় করা হয়। সেই জটিলতায় যাব না। এবার যোগ দেখাচ্ছি সেটা দ্যাখো”
বলে উঠে আবার একতাড়া কাগজ নিয়ে এলেন গোপালচন্দ্র। “ইদানীং ল্যাবরেটরিতে বিশেষ থাকি না, মাঝেমধ্যে বেরিয়ে যাই। কোথায় যাই জানো?”
“না। আমার জানার এক্তিয়ার নেই।”
“আছে আছে। নাম শুনলেই বুঝবে আছে। এমন এক জায়গায়, যেখানে কিছু বছর আগে মাস্টার তোমায় কাজ দিয়েছিলেন পাগল ধরে আনার।”
“ডালান্ডা!! আবার পাগলদের…”
“না না, এবার তেমন নৃশংস কিছু হচ্ছে না। আমি শুধু আমার বড়ির উপযোগিতা দেখতে গেছিলাম।”
“কাজ হচ্ছে?”
“হচ্ছে। প্রয়োগের ঠিক আধ ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টার মধ্যে। এই সময়টা মানুষে মানুষে আলাদা হয়। কিন্তু কাজ হচ্ছে। ওষুধের প্রভাবে আর দুটো ঘটনা ঘটে। রোগীর দেহের তাপমাত্রা অত্যধিক বেড়ে যায় আর হাতের তালু খসখসে হয়ে ঘাম হতে থাকে। সেই দেখেই কিছুদিন আগে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। আর এই দ্যাখো। ক্যাপসুল খাওয়ানোর আগের আর পরের আঙুলের ছাপ। কী বুঝছ?”
লখনের মুখ না চাইতেই হাঁ হয়ে গেল।
“এ তো সব লুপ আর্চ হয়ে গেছে!”
“এক্সজ্যাক্টলি। সেই আর্চ, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে সবচেয়ে রেয়ার। যদিও ওষুধের প্রভাব কমলে ছাপ আপনাআপনি আগের মতো হয়ে যায়, তবুও এ জিনিস কী ভয়ানক একটা দিক খুলে দিল বুঝতে পারছ?”
“বোধহয় পারছি।”
“কিচ্ছু পারছ না। অপরাধীকে শনাক্ত করার জন্য একেবারে পাথুরে প্রমাণ এই হাতের ছাপ। সবাই জানে হাতের ছাপ বদলানো যায় না। কিন্তু খানিকক্ষণের জন্য হলেও যদি হাতের ছাপ বদলে যায়, তবে কী জঘন্য সব ঘটনা ঘটতে পারে ভেবেছ কোনও দিন? অপরাধী অপরাধ করে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে। চাক্ষুষ প্রমাণ থাকলেও ধরার উপায় থাকবে না। এত অসামান্য একটা অস্ত্র একেবারে ভোঁতা হয়ে যাবে। আর দুটো অদ্ভুত ব্যাপার আছে…”
“কী?”
“ভূতের প্রয়োগের মাত্রা একেবারে সঠিক না হলে ভূত প্রয়োগকারীকে ও ছাড়ে না, আর যার উপরে ভূত প্রয়োগ হচ্ছে, প্রভাব কেটে গেলে সে প্রয়োগের পূর্বের বহু কথাও বিস্মৃত হয়। আমার বিশ্বাস আমার গবেষণায় আমি এই ত্রুটি দূর করতে পারব। তার জন্য সময় লাগবে। মাস্টার ম্যাসন জানলে সে সময় আমাকে দেবেন না। ওঁর কাজ শেষ, কিন্তু আমার গবেষণা সম্পূর্ণ হয়নি। তোমায় বিশ্বাস করে বললাম। তুমি এখনই দয়া করে কাউকে এটা জানিয়ো না। মাস্টার ম্যাসনকেও না।”
“কথা দিলাম”, লখন বলল।
পরের দিন ল্যাবরেটরিতে ঢোকার আগেই গেটে দারোয়ান জানাল ডিরেক্টর সাহেব গোপালচন্দ্রকে ডেকেছেন। গোপাল একটু অবাক হলেন। স্বয়ং ডিরেক্টর তলব করেছেন! গুরুতর কিছু ঘটল নাকি? ডিরেক্টরের ঘরে যেতেই তিনি গোপালকে জানালেন, অনিবার্য কারণবশত গোপালচন্দ্রকে আর ক্যানিংহ্যাম ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে দেওয়া যাবে না। শুধু তাই না, বিশেষ কারণে কেউ, এমনকি গোপালচন্দ্রও আবার অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত সেই গবেষণাগারে প্রবেশ করতে পারবেন না। তাঁকে আবার মেডিক্যাল কলেজে ফিরে যেতে হবে। আগের মতোই সার্জারির কাজ করতে হবে। প্রায় তিন বছর সেই ল্যাবরেটরিতে ঠিক কী হল কেউ জানে না। কয়েক বছর বাদে, ১৮৯৮ সালে বম্বে ফেরত এক খিটখিটে বদরাগি সাহেব ডাক্তার কালাজ্বর আর ম্যালেরিয়া নিয়ে কাজ করতে সেই গবেষণাগারে এলেন। ডাক্তারের নাম রোনাল্ড রস।
.
৬।
পঞ্চদশ শতকে পর্তুগিজরা বাংলায় এসে দুটো নৌবন্দর দেখতে পায়। বড়োটি চট্টগ্রামে আর ছোটোটি আদিসপ্তগ্রামে, যার পর্তুগিজ নাম ছিল পোর্টো পিকোনো। ছোটো বন্দর। আদিসপ্তগ্রামে সমস্ত উত্তর ভারত থেকে পণ্য আসত। নদীতে নৌকার ছড়াছড়ি। কিন্তু নদীর গতিপথ বদলানোয় ক্রমশ চড়া পড়তে পড়তে একসময় আদিসপ্তগ্রাম বন্দর হিসাবে পরিত্যক্ত হয়। একই দশা হয় হুগলিরও। এদিকে আদিগঙ্গার ধারাও ক্রমশ তার নাব্যতা হারিয়ে কালো পচা জলের নালায় পরিণত হয়। অগত্যা উপায় না দেখে পর্তুগিজদের বড়ো বড়ো জাহাজগুলো নদীর আরও দক্ষিণে নাব্য এলাকায় নোঙ্গর ফেলত। অন্য পাড়ে শিবপুরের কাছে বেতড়ে তৈরি হল বিদেশিদের বাজার। বাজারের কেনা-বেচার বহর দেখে আকৃষ্ট হয়ে আদিসপ্তগ্রাম ছেড়ে চারটি নেটিভ বসাক পরিবার ও এক শেঠ পরিবার নদীর এপাড়েই গোবিন্দপুরে বাসা বাঁধে। বেতড়ের উলটো দিকে নতুন বাজার গড়ে ওঠে। নাম হয় সুতানুটি। সে অনেক কাল আগের কথা। ইংরেজরা এসে নদীর ধারে খোলামেলা এই জায়গার নাম দিয়েছিলেন গার্ডেনরিচ। সারাদিনের গরমে ক্লান্ত হয়ে সবাই সন্ধেবেলা হাওয়া খেতে আসতেন নদীর পারে।
এখন অবশ্য সেদিন আর নেই। ওই এলাকাতেই কলকাতা বন্দর গড়ে উঠেছে আর বন্দরকে কেন্দ্র করে নানা কলকারখানা। আগে বাংলায় চটকল ছিল না। ছিল সেই ডান্ডিতে। যদিও কাঁচামাল বয়ে নিয়ে যেতে হত এই বাংলা থেকেই। চতুর ইংরেজ আর স্কট ব্যবসায়ীরা দেখলেন এর চেয়ে গঙ্গার ধারে এই কলকাতার আশেপাশেই কল বানালে খরচা অনেক কম, মুনাফা বেশি। একে একে চটকল গড়ে উঠেছে কাঁকিনাড়া, বজবজ আর গার্ডেনরিচে। সাহেবরা এই মিলগুলো নিজেরা চালান না। চালান দেশি এজেন্সি মারফত। ফলে দেশি সদাগর আর বিদেশি শিল্পপতি মিলে লাভের গুড় খান আর মরে চটকলের সাধারণ শ্রমিকরা। গত তিন বছর যাবৎ প্রায়ই মালিকদের সঙ্গে শ্রমিকদের বচসা বাধছে। শুরুতে গণ্ডগোল আয়ত্তে থাকলেও বকরি ইদের দিন কাঁকিনাড়া চটকলে বাড়াবাড়ি রকমের ঝামেলা হল। বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ল আশেপাশের চটকলগুলোতেও। কিন্তু গার্ডেনরিচে এই গণ্ডগোলের আঁচ পড়তে দেননি মালিক মাইকেল স্টুয়ার্ট। তিনি নিজে চটকল চালান। এজেন্সির মাধ্যমে না। ফলে শ্রমিকরা কিছু হলেও বেশি পারিশ্রমিক পায়। তাদের কোনও ক্ষোভ নেই। অক্ষত স্টুয়ার্ট নিজে তেমনটাই ভাবতেন।
সেদিনও সকাল থেকে রোজকার মতোই কাজ শুরু হল। ফোরম্যান বুড়ো আবুল হাসান কলের বাঁশিতে সময়মতো ভোঁ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল চারিদিকের তদারক করতে। বাইরে থেকে সব স্বাভাবিক মনে হলেও আবুলের মনে কেমন কু ডাকছে। অন্যদিন সবাই ছড়িয়েছিটিয়ে নিজেদের মতো কাজ করে। আজ চার-পাঁচজন মিলে জটলা বেঁধে এক-এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কী যেন আলোচনা করছে। আবুল কাছে গেলেই চুপ মেরে যাচ্ছে। আবুলের অস্বস্তি শুরু হল। বছরখানেক আগে বেহার মুলুক থেকে শিউচরণ দুবে এই চটকলে যোগ দেবার পর থেকেই কারখানার পরিবেশ কেমন যেন বদলে গেছে। শিউচরণ একটু নেতা গোছের। বয়স কম। রক্ত গরম। সে মাঝে মাঝেই সবাইকে বোঝায় মালিক তাদের কতটা ঠকিয়ে মুনাফা কামাচ্ছে। আবুলকেও বোঝাতে এসেছিল। আবুল ভাগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু অন্য মুসলমান শ্রমিকরা তার কথা মন দিয়ে শোনে। এসব কথা শোনাও গুনাহ। যে মালিক তাকে খাইয়ে পরিয়ে রেখেছে, যার দয়ায়তার বউ, পাঁচ ছেলেমেয়ে বেঁচে আছে, তার নামে এসব না-পাক কথা শুনলে দোজখেও ঠাঁই হবে না। এখন সে শিউচরণের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু বুঝতে পারে ভিতরে ভিতরে শিউচরণ ঘোঁট পাকাচ্ছে। যে-কোনো দিন এই কলেও একটা গণ্ডগোল বাধবে। একবার ভাবে সে সাহেবকে সব বলে দেবে। তারপরেই ভাবে, বললেই সাহেব বলবে সন্দেহের তালিকায় কে কে আছে, তাদের নাম বলতে। আর নাম বললেই সাহেব তাদের চাকরি খাবে। সেটাও ঠিক না। এক হপ্তা হল কোথা থেকে ভাইপোকে এনে জুটিয়েছে। সে আবার দারোয়ানের কাজ করে। এদের কী মতলব কে জানে? অতএব চোখকান খোলা রেখে চলে সে। আজকেও চলছিল। আর চলতে চলতেই প্রথমবার ছেলেটাকে চোখে পড়ল তার।
কুচকুচে কালো চেহারা। মাথায় পাতা কেটে আঁচড়ানো তেল চকচকে চুল। খাটো ধুতি পরা। চটকাটার মেশিনে জোরে ঘোরা চাকার পাশে দাঁড়িয়ে পাটের গুছি ঢোকাচ্ছে। আগে এই ছেলেকে কোনও দিন দেখেনি আবুল। একটু আগ্রহী হয়েই তার কাছে এগিয়ে গেল। ছেলেটা দূর থেকেই তাকে দেখতে পেয়ে একটা সেলাম ঠুকে দাঁড়াল। যাক! সহবত জানে অস্তত। আর তখনই আবুল খেয়াল করল ছেলেটার কড়ে আঙুলের কিছুটা নেই।
“নাম কেয়া হ্যায় তেরা?” প্রশ্ন শুনে আবুলের মুখের দিকে ফ্যালফেলিয়ে চেয়ে রইল ছেলেটা। আবুল বুঝল নেহাত গাঁয়ের ছেলে। সদ্য কলকাতা এসেছে। হিন্দি জানে না।
“নাম… কী নাম আছে তোর?”
“এজ্ঞে ভবতারণ জানা, এজ্ঞে”, দুই হাত জোর করে মাটির দিকে চেয়ে মিনমিন করে বলল ছেলেটা।
“ঘর কোথা আছে?”
“এজ্ঞে, গাঁয়েরবাড়ি মিদনাপুরের বালিচকে।”
“তাহলে ইখানে কী করছিস?”
“এজ্ঞে, কায়েতের ছেলে। পড়াশুনো কিছু হলনি। বাবা বললে কলকেতায় গে দেখ যদি কিছু হয়। তা গাঁয়ের বিপিন মাইতিকে বলতে সে এই কলে টেনির কাজে ঢুকিয়ে দিলে। এক আনা রোজ।”
“ঠিক হ্যায়। মন দিয়ে কাজ শিখে নে”, বলে বাইরে বেরোতেই শিউচরণকে আবার দেখতে পেল আবুল। গেটের সেই দারোয়ান ভাইপোর সঙ্গে ফিসফিস করে কী যেন বলছে আর আবুলকে আড়চোখে দেখছে….
দুপুরে খাবারের ঘন্টা পড়লে যোহরের নমাজ সেরে ওজু করে খেতে বসতে যেতেই আবার ছেলেটার দিকে চোখ পড়ল আবুলের। ছেলেটার মুখ বড়ো মায়াভরা। চোখ দুটো বড়ো, টানা টানা। এক কোণে চুপচাপ বসে আছে। সামনে খাবারদাবার কিছু নেই। হাতছানি দিয়ে ডাকল আবুল, “এ ভবতারণ, ইধার আ।”
বুঝতে পেরে গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে এল ছেলেটা।
“কুছু খাবার আনিসনি?”
উত্তর না দিয়ে পাশাপাশি মাথা নাড়ল, চোখ মাটির দিকে।
“কেন আনিসনি? কিনার পয়সা নেই?”
আবার সে আগের মতোই মাথা নাড়ল। আবুলের মনে হল চোখের কোনায় যেন জল চিকচিক করছে। ধর্মপ্রাণ মুসলমান আবুল কাউকে অভুক্ত রেখে খেতে পারে না। কিন্তু এ কি তার হাতের ছোঁয়া খাবে? জিজ্ঞাসা করতে এককথায় রাজি হল ছেলেটা। রুটি আর সবজি আবুল ভাগ করে নিল তার সঙ্গে। কিন্তু জল? তার ঘাটির জল খাইয়ে সে এই ছেলের জাত মারবে না। ছেলেটা যখন বুভুক্ষুর মতো খাচ্ছিল, তখন একফাঁকে সে উঠে গেল জলের পাত্রের সন্ধানে। সেই সামান্য সময়ে ছেলেটার বাঁ হাত চলে গেল ফতুয়ার পকেটে। বেরিয়ে এল ছোটো একটা কাচের ডিবে, আর তাতে ভর্তি সাদা সাদাবড়ি। সবার অলক্ষে একটা বড়ি আবুলের ঘটির জলে মিশতেই সামান্য ফিসস আওয়াজ করে গুলে গেল। মাটির খুরিতে জল ভরে আবুল যখন ফিরে এল তখন ছেলেটার খাওয়া সবে শেষ হয়েছে। একগাল হেসে সে পাত্রটা আবুলের থেকে নিয়ে ঢকঢক করে একেবারে গোটা জলটা খেয়ে নিল। আবুল নিজেও ঘটির জল পুরোটা শেষ করে একটা কাপড় দিয়ে মুছে নিল মুখ, মাথা, ঘাড়। এখনও হাতে খানিক সময় আছে। বিপিন মাইতি না কার একটা নাম বলল ছেলেটা, সে নাম আগে কোনও দিন শোনেনি আবুল। কোন ডিভিশনে কাজ করে কে জানে? ছেলেটাকে সবে জিজ্ঞেস করতে যাবে, আর তখনই আবুলের কানে এল আওয়াজটা। একটা হইহই আওয়াজ কোথা থেকে আসছে যেন…. ভিতরের গেটের একপাশে শিউচরণের সেই ভাইপো দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখছে। আর কোনও দিকে খেয়াল না করে আবুল সব ফেলে তড়িঘড়ি ছুট লাগাল আওয়াজের উদ্দেশে।
.
মাইকেল স্টুয়ার্ট কারখানার মেইন গেট বন্ধ করার আদেশ দেবার ঠিক আগে ক্ষিপ্র বিড়ালের মতো লখন সবার অলক্ষে কারখানা থেকে বেরিয়ে গেল। আবুল ততক্ষণে হাসি হাসি মুখে দৃঢ় হাতে শিউচরণের ভাইপো কানাইয়ালালের টুটি টিপে ধরেছে…
.
৭।
“ভিতরে এসো ল্যানসন। সামনে এসে বোসো। কাজ চলছে?”
“হ্যাঁ, মাস্টার।”
“জানি। আমার কানেও খবর এসেছে। ব্রাদারহুডের সৈনিক হিসেবে তুমি যা করছ, তা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে।”
“ধন্যবাদ মাস্টার।”
“ভূতের কার্যকারিতা কেমন?”
“যেমন আন্দাজ করা গেছিল তেমন।”
“সে তো হবেই ল্যানসন, সে তো হবেই। কিন্তু যেটা আসল কথা, প্রয়োগের পরে কাজ হতে কত সময় লাগছে?”
“সেটা দেখার জন্যেই তো এই পরীক্ষাগুলো করছি মাস্টার। তবে এতদিনে বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন মানুষের উপরে ব্যবহার করে একটা জিনিস বোঝা গেছে, এই বড়ি কাজ করতে কুড়ি মিনিট থেকে দেড় ঘণ্টা অবধি সময় নেয়।”
“কার ক্ষেত্রে কত নেবে সেটা বোঝার উপায় আছে?”
“হয়তো আছে। সবচেয়ে কম সময় লেগেছিল গার্ডেনরিচে, কুড়ি মিনিট। সবচেয়ে বেশি সেই কিলবার্ন কোম্পানির ইলেকট্রিক মিস্তিরির বেলায়। আমি প্রায় হাল ছেড়েই দিয়েছিলাম। পরে বুঝলাম গোটাটাই ওজনের উপরে নির্ভর করে। যার ওজন যত বেশি, তার ক্ষেত্রে এই বড়ির কাজ হয় তত দেরিতে। গার্ডেনরিচের আবুল ছিল রোগাপাতলা লোক, কিন্তু কিলবার্নের সেই…..”
“বুঝেছি। খুব ভালো। এবার তোমাকে কয়েকটা জরুরি কথা বলছি। মন দিয়ে শোনো।”
“বলুন মাস্টার।”
“এতদিন নানা জায়গায়, নাম ভাঁড়িয়ে ছদ্মবেশে তুমি যে কাজগুলো করেছ, ব্রাদারহুড তার জন্য তোমার কাছে ঋণী। কিন্তু আজ এই মুহূর্ত থেকে তোমার সেসব কাজ বন্ধ। আবার লুকিয়ে পড়ো। যেন কেউ আর তোমায় না দেখতে পায়।”
“কিন্তু কেন মাস্টার?”
“তুমি জানো না, নাকি জেনেও অস্বীকার করছ যে তোমার পিছনে পুলিশ লেগেছে?”
“প্রিয়নাথ দারোগা?”
“সে তো আছেই। সঙ্গে বিলেত থেকে আসা এক ধুরন্ধর গোয়েন্দা সাইগারসন-ও রয়েছে। তুমি এদের চেনো?”
“হ্যাঁ। ডালান্ডায় দেখেছিলাম। তখন চিনতাম না। নাম ভাঁড়িয়ে এসেছিল। পরে চিনেছি।”
“তারা হন্যে হয়ে তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে।”
“কিন্তু আমায় কেন?”
“দলের মধ্যেই কেউ একজন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তোমার পরিচয় ওদের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছে।”
“কে সে?”
“আমাদের একজনকে সন্দেহ ছিল। খুব সম্ভব সে-ই।”
“নামটা বলুন…”
“তুমি তো বাংলা পড়তে পারো। দ্যাখো দেখি, এই নাটকটা চেনো?”
“এটা তো…. কিন্তু শৈল শপথ নিয়েছিল জীবনে আর নাটক লিখবে না। ও এ কাজ করবে কেন?”
“করবে শুধু না, করেছে। তুমি বিজ্ঞাপন অংশের প্রতি প্যারার প্রথম শব্দের প্রথম অক্ষরগুলো মিলিয়ে দ্যাখো।”
“বি-ক-তো-রি-আ! সে কী!!”
“শুধু তাই না, আমাদের গোটা প্ল্যানের কথা সাঁটে এই নাটকে লেখা আছে।”
“কিন্তু কেন? ব্রাদার শৈলর মতো মানুষ … শৈল কী বলছে?”
“সে কিছু বলার জায়গায় নেই। ওরা শত্রুর শেষ রাখেনি। কাল রাতে শৈল চুঁচুড়ায় এসেছিল, ওখানেই ওকে খুন করা হয়। মৃতদেহ সকালে উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু সেটা বড়ো কথা না। খুন করা হয়েছে একেবারে টেক্সটবুক জাবুলনদের পদ্ধতিতে। পেট চিরে দুই ফালা, মুখে অণ্ডকোশ কেটে ঢোকানো।”
“তবে কি ব্রাদারহুডেরই কেউ…..”
“আমার আদেশ ছাড়া ব্রাদারহুডের কারও সাধ্যি হবে না শৈলর গায়ে হাত দেবার। এ কাজ বাইরের কেউ করেছে। প্রমাণ লোপাট। আর যদি তাই হয়, তবে বিপদটা বুঝতে পারছ? এ এমন কেউ যে আমাদের ভিতরের সবরকম খবর রাখে, আর শুধু রাখেই না, এইভাবে খুন করে ব্রাদারহুডকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করতে পারে।”
“কোনও ধারণা করেছেন সে কে হতে পারে? প্রিয়নাথ বা সাইগারসন?”
“এঁরা সজ্জন মানুষ। আইন নিজের হাতে নেবার লোক নন। একটা নাম …”
“কী নাম?”
“একটা নাম ঘুরে বেড়াচ্ছে বাতাসে। অশরীরীর মতো। ম্যানুয়েল ডিব্যাসি। সে যে কে, কোথা থেকে কী উদ্দেশ্য, কিছুই এখনও জানা যায়নি। আমরা খোঁজ চালাচ্ছি। কিন্তু সবার আগে দরকার তোমার একেবারে লুকিয়ে পড়া। শৈলর ঘটনার পরে আমি আর কোনও ঝুঁকি নেব না। তোমরা তিনজন কিডস্ট্রিটের বাড়ি ছেড়ে ব্রাদারহুডের মূল বাড়িতে চলে এসো। আমার আদেশ।”
“কিন্তু মাস্টার, একেবারে অশরীরী একজনের জন্য…”
“দাঁড়াও দাঁড়াও! তোমাকে তবে একটা জিনিস দেখাই। এই ব্রোমাইড ফটোতে একজনকে রাজভবনের বাইরে দেখা যাচ্ছে, দ্যাখো দেখি তাকে চেনো কিনা?”
“এ কী!! কিন্তু আমিতো…”
“জানি। তোমার অজ্ঞাতেই এই ছবি তোলা। হীরালাল সেন নামে এক শখের ফটোগ্রাফার রাস্তাঘাটের ছবি তোলে। তার ক্যামেরাতেই তোমার এই ছবি বন্দি হয়েছে। শুধু হয়নি, লালমোহন মল্লিকের বাড়িতে পর্দা টাঙিয়ে দেখানোও হয়েছে। দর্শকদের মধ্যে আমাদের এক ব্রাদার ছিলেন। তিনি চড়া দামে ছবিটা কিনে নেন। কিন্তু এর কোনও কপি আছে কিনা আমাদের জানা নেই। তাই তুমি এখন অচেনা না। পুলিশের হাতে এই ছবি এলে কী হতে পারে ভেবেছ? কিংবা সেই খুনির হাতে?”
“তবে আমার কী কর্তব্য?”
“সবার আগে দ্রিনা আর মারিয়ানার সুরক্ষা। তারপর তোমার সুরক্ষা।”
“আর আমার কাজ?”
“অন্য কেউ করবে। তোমাকে আর যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে দেওয়া যাবেনা। এমনকি তোমার কাছে যে বাক্সটা গচ্ছিত আছে সেটাও কিছুদিনের জন্য অন্য কাউকে দিতে হবে। মুশকিল হল তেমন যোগ্য লোক পাওয়া মুশকিল।”
“আমার একটা কথাছিল।”
“বলে ফেলো।”
“একজন আছে। হাতসাফাইয়ের কাজে আমার চেয়েও দড়। সত্যি বলতে ভোজবাজি আমরা একই গুরুর থেকে শিখেছিলাম।”
“অ্যাংলো? খ্রিস্টান?”
“নাহ। হিন্দু ব্রাহ্মণের ছেলে। তিনকূলে কেউ নেই। আমার কথা বেদবাক্যের মতো মানে।”
“কীকরে?”
“জাদুর খেলা দেখিয়ে বেড়ায়। আগে রাস্তায় দেখাত। এখন ধনী মানুষদের বাড়ি গিয়ে গিয়ে দেখায়।”
“বিশ্বাস করা যায়?”
“চোখ বুজে। সত্যি কথা বলতে কি, আমিও চাইছিলাম ওর সঙ্গে আবার যোগাযোগ করতে। আজ রাতেই ওর আস্তানায় আসার কথা।”
“তাও একবার পরীক্ষা করে নাও। দরকার হলে ওকে আমাদের ব্রাদারহুডে নিয়ে এসো। ব্রাদারহুডের অনুশাসনে না এলে তাকে কোনও কাজের দায়িত্ব দেওয়া যাবেনা।”
“একেবারেই সহমত মাস্টার।”
“আর দেখো, কোনওমতে দলের বাকিদের নাম, আমার নাম ইত্যাদি যেন এর কাছে প্রকাশ না পায়।”
“তাই হবে মাস্টার।”
“তবে কাজ শুরু করে দাও। সময় নেই। মাত্র কয়েকমাস। তারপরেই… কী নাম তোমার এই জাদুকর বন্ধুর?”
“গণপতি। গণপতি চক্রবর্তী।”