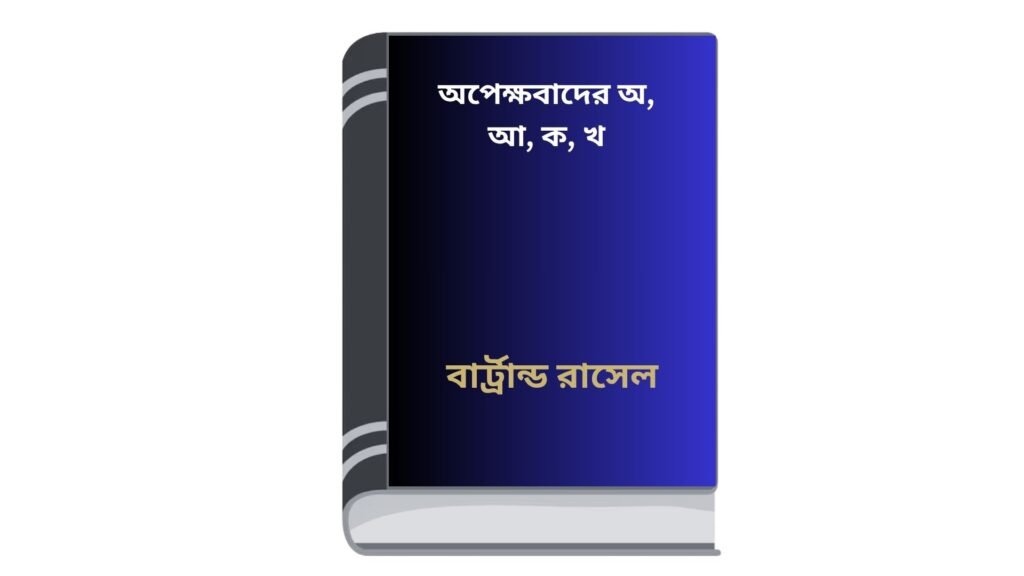১২. প্রচলিত রীতি এবং প্রাকৃতিক বিধি
১২. প্রচলিত রীতি এবং প্রাকৃতিক বিধি
যেকোনো বিতর্কে শব্দ (word) বিষয়ক দ্বন্দ্ব এবং বাস্তব ঘটনা (facts) বিষয়ক দ্বন্দ্ব পৃথক করা কঠিনতম বিষয়গুলির ভিতর একটি। কঠিন হওয়া উচিত না হলেও কার্যক্ষেত্রে ব্যাপারটা কঠিন। এ তথ্য অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে যেমন সত্য তেমনি সত্য পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে। সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রচণ্ড বিতর্ক হয়েছিল : ‘বল’ (force) কাকে বলে তাই নিয়ে। এখন আমাদের কাছে এটা স্বতঃপ্রতীয়মান যে তর্কটা ছিল বল (force) শব্দটা কি করে সংজ্ঞিত (defined) হবে তাই নিয়ে। কিন্তু সে কালের চিন্তন ছিল : বিতর্কের বিষয়টা এর চাইতে অনেক বড়। অপেক্ষবাদের গণিতে টেন্সর (tensor) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। টেন্সর পদ্ধতি ব্যবহারের একটি উদ্দেশ্য ছিল ভৌতিবিধি (physical laws) থেকে শুদ্ধ শাব্দিক (purely verbal)-কে (বিস্তৃত অর্থে) বিযুক্ত করা। এটা অবশ্য স্বতঃপ্রতীয়মান যে স্থানাঙ্ক নির্বাচনের উপর যা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট অর্থে সেটা শাব্দিক (verbal)। একটি লোক লগি ঠেলে নৌকা বরাবর হাঁটছে কিন্তু লগিটা না তোলা পর্যন্ত সে নদীতল সাপেক্ষ তার অবস্থান অপরিবর্তিত রাখছে। যে লোকটা লগি ঠেলছে সে হাঁটছে না স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এ নিয়ে একজন লিলিপুট সীমাহীন তর্ক করতে পারে। তর্কটা হবে শব্দ বিষয়ে বাস্তব ঘটনা বিষয়ে নয়। আমরা যদি নৌকা সাপেক্ষ স্থির স্থানাঙ্ক নির্বাচন করি তাহলে লগি ঠেলা লোকটা হটছে আর যদি নদীতল সাপেক্ষ স্থির স্থানাঙ্ক নির্বাচন করি : তাহলে লগি ঠেলা লোকটি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ভৌতবিধি আমরা এমনভাবে প্রকাশ করতে চাই যাতে দুটি বিভিন্ন স্থানাঙ্কতন্ত্রে আরোপ করলেও আমরা এই বিধি প্রকাশ করছি এটা স্বতঃপ্রতীয়মান হবে। তাহলে যখন আমরা একটি মাত্র বিধি ভিন্ন বাগ্বিধিতে প্রকাশ করছি তখন ভুলক্রমেও অনুমান করব না যে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন বিধি রয়েছে। এ কাজ করা যায় টেন্সর পদ্ধতিতে। কতগুলি বিধি একটি ভাষায় সম্ভাব্য মনে হলেও অন্য ভাষায় অনুবাদ করা যায় না। প্রাকৃতিক বিধিরূপে এগুলি গ্রহণ করা সম্ভব নয়। যে বিধিগুলি যে কোনো স্থানাঙ্কের বাগ্বিধিতে অনুবাদ করা সম্ভব সে বিধিগুলির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। অপেক্ষবাদ যেগুলিকে সম্ভাব্য মনে করে, প্রাকৃতিক বিধিগুলির ভিতর থেকে সেগুলি খুঁজতে হলে এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রচুর সাহায্য করে। সম্ভাব্য বিধিগুলির ভিতরে যেগুলি বস্তুপিণ্ডের সত্যকার গতি সম্পর্কে নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করে সেগুলির ভিতরে সরলতম বিধিই আমরা নির্বাচন করি। এই নির্বাচনের যুক্তি এবং অভিজ্ঞতা সমপরিমাণে সাহায্য করে।
কিন্তু সত্যকারের প্রাকৃতিক বিধি প্রাপ্তির সমস্যা শুধুমাত্র টেন্সর পদ্ধতির দ্বারাই সমাধান করা যাবে না। তার সঙ্গে প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণ সতর্ক চিন্তন। এর ভিতরে খানিকটা করা হয়েছে কিন্তু অনেকটাই বাকী আছে।
একটি সরল উদাহরণ : অনুমান করা যাক একটি অভিমুখের দৈর্ঘ্য অন্য অভিমুখের দৈর্ঘ্যের তুলনায় কম অর্থাৎ লোরেঞ্জ সঙ্কোচনের প্রকল্পে যে রকম আছে সেইরকম। ধরে নেওয়া যাক উত্তর অভিমুখী একটি ফুটরুলের দৈর্ঘ্য পূর্বমুখী একই ফুটরুলের দৈর্ঘ্যের অর্ধেক এবং এ তথ্য সমস্ত বস্তুপিণ্ড সাপেক্ষই সত্য। এইরকম প্রকল্প কি অর্থবহ? আপনার একটি মাছ ধরার ছিপ পশ্চিমমুখী ঘোরালেও তার দৈর্ঘ্য যদি পনের ফুট হয়, সেটা উত্তরমুখে ঘোরালেও তার দৈর্ঘ্য পনের ফুটই থাকবে। তার কারণ মাপনদণ্ডটিও হ্রস্ব হয়ে যাবে। এটা হ্রস্বতর দেখাবে না কারণ আপনার চক্ষুও প্রভাবিত হবে একই ভাবে। পরিবর্তনটা যদি খুঁজে বার করতে চান তাহলে সাধারণ মাপনে চলবে না। এর জন্য চাই মিচেলসন-মর্লি পরীক্ষার ধরনের কোনো পদ্ধতি। মিচেলসন-মর্লি পরীক্ষায় আলোকের বেগকে দৈর্ঘ্য মাপার জন্য ব্যবহার করা হয়। তারপরও দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন অনুমান করা সহজতর, না আলোকের বেগের পরিবর্তন অনুমান করা সহজতর, এ বিষয়ে আপনাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। পরীক্ষামূলক তথ্য হবে; আপনার ফুটরুল যে দূরত্ব নির্দেশ করে সে দূরত্ব অতিক্রম করতে এক অভিমুখের চাইতে অন্য অভিমুখে আলোকের বেশি সময় লাগছে কিংবা মিচেলসন-মর্লি পরীক্ষার মতো : বেশি সময় লাগা উচিত কিন্তু লাগছে না। এই রকম তত্যের সঙ্গে আপনার মাপনকে আপনি নানা ভাবে মানিয়ে নিতে পারেন। যে পদ্ধতিই আপনি গ্রহণ করুন না কেন চলতি রীতির খানিকটা তার ভিতরে থাকবে। মাপন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আপনার বিধিগুলি গঠনের পরও এই চিরাচরিত রীতির খানিকটা থেকে যায়। অনেক সময়ই এ অস্তিত্বের রূপ সূক্ষ্ম এবং কপট (elusive)। চিরাচরিত রীতিকে বিযুক্ত করা আসলে অসাধারণ কঠিন ব্যাপার। ব্যাপারটা যত বিবেচনা করা যায় কাঠিন্য ততই বেশি মনে হয়।
ইলেকট্রনের আকারের প্রশ্ন আরো গুরুত্বপূর্ণ একটি উদাহরণ। পরীক্ষায় দেখা যায় সমস্ত ইলেকট্রনের একই আকার, এর কতটা পরীক্ষালব্ধ অকৃত্রিম বাস্তব সত্য এবং কতটা মাপনের চিরাচরিত রীতির ফলস্বরূপ, এ ক্ষেত্রে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন দুটি তুলনা করতে হয় : (১) বিভিন্ন কালে একটি ইলেকট্রন বিষয়ে, (২) একই কালে দুটি ইলেকট্রন বিষয়ে। তারপর আমরা প্রথমটির সঙ্গে দ্বিতীয়টিকে সংযুক্ত করে বিভিন্ন কালে দুটি ইলেকট্রনের তুলনা করতে পারি। সমস্ত ইলেকট্রনকে একইভাবে প্রভাবিত করবে এরকম প্রকল্প আমরা পরিত্যাগ করতে পারি। উদাহরণ : একটি স্থান-কাল অঞ্চলের সমস্ত ইলেকট্রন অন্য একটি স্থান-কাল অঞ্চলের সমস্ত ইলেকট্রনের চাইতে বড় এইরকম কোনো প্রকল্প। এই রকম কোনো পরিবর্তন আমাদের মাপন যন্ত্র এবং মাপিত বস্তুকে সমানভাবে প্রভাবিত করবে সুতরাং আবিষ্কারযোগ্য কোনো পরিঘটনা এর ফলে পাওয়া যাবে না। এ কথা বলা এবং কোনো পরিবর্তন হবে না বলা সমার্থক। কিন্তু উদাহরণস্বরূপ বলা যায় : দুটি ইলেকট্রনের একই ভর এই বাস্তব ঘটনাকে শুদ্ধ রীতিগত বলা যায় না। যথেষ্ট সূক্ষ্মতা এবং নির্ভুলতা থাকলে, তৃতীয় একটি ইলেকট্রনের উপর দুটি ইলেকট্রনের ক্রিয়ার তুলনা আমরা করতে পারি। সমরূপ পরিবেশে যদি তারা অভিন্ন হয় তাহলে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি অভিন্নতা শুধুমাত্র শুদ্ধ রীতিগত নয়।
অপেক্ষবাদের উচ্চতর পর্যায়ের (advanced portions) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পদ্ধতিকে এডিংটন বিশ্বগঠন’ (World Buildings) আখ্যা দিয়েছিলেন। যে অবয়ব গঠন করতে হবে সেটা হল আমাদের জানা ভৌত বিশ্ব। হিসাবী স্থপতি চেষ্টা করেন সম্ভাব্য স্বল্পতম সামগ্রীর সাহায্যে গঠন করতে। এটা যুক্তি আর গণিতের প্রশ্ন। এই দুই বিষয়ের প্রযুক্তিতে আমাদের দক্ষতা যত বেশি হবে অবয়বের গঠনও হবে তত বেশি বাস্তব এবং শুধুমাত্র পাথরের স্থূপে আমাদের সন্তুষ্টি তত কমবে। কিন্তু প্রকৃতি আমাদের যে পাথরগুলি দিয়েছেন অবয়ব গঠনের আগে সেগুলিকে সঠিক আকারের কাটতে হবে। এ সমস্তই গঠনক্রিয়ার অংশ। এ কাজ সম্ভব হতে হলে কাঁচালেরও গঠন থাকা প্রয়োজন [একে আমরা কাঠের জমিনের (grain) সদৃশরূপে কল্পনা করতে পারি। কাজ কিন্তু প্রায় যে কোনো গঠনেই চলবে। পারস্পরিক গাণিতিক পরিমার্জনার সাহায্যে আমাদের প্রাথমিক প্রয়োজনকে ছাঁটকাট করে কমাতে থাকি। শেষ পর্যন্ত তার পরিমাণ থাকে অতি অল্প। প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন এই গঠন (grain) কাঁচামালে থাকলে আমরা দেখতে পাই–তা থেকে আমরা এমন একটি গাণিতিক অভিব্যক্তি গঠন করতে পারি, যে অভিব্যক্তির আমাদের অনুভূত বিশ্বের বিবরণ দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় গুণ থাকবে। বিশেষ করে থাকবে নিত্যতা ধর্মের বিবরণ দেওয়ার মতো গুণ। এই ধর্মই ভরবেগ এবং শক্তির (কিংবা ভরের) বৈশিষ্ট্য। শুধুমাত্র ঘটনাগুলি ছিল আমাদের কাঁচামাল। কিন্তু যখন দেখতে পাই এর সাহায্যে আমরা এমন কিছু গঠন করতে পারি যা কখনো সৃষ্টি হয়েছে কিংবা ধ্বংস হয়েছে বলে প্রতিভাত হয় না তখন আমরা বস্তুপিণ্ডে’ বিশ্বাস করতে শুরু করি–এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। এগুলি আসলে ঘটনা থেকে তৈরি গাণিতিক গঠন, কিন্তু স্থায়িত্বের (premanence) দরুন সেগুলির ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে। আমাদের বোধেন্দ্রিয়গুলি (হয়তো জৈব প্রয়োজনই সেগুলির বিকাশের কারণ) তাত্ত্বিক দিক দিয়ে অধিক মূলগত কিন্তু অমার্জিত (crude) অবিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীর স্থলে সেগুলি লক্ষ্য করার জন্য অভিযোজিত (adopted)। তবে তাত্ত্বিক দিক থেকে অমার্জিত অবিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীই বেশি মূলগত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ভৌত বিজ্ঞান বাস্তব বিশ্বের কত সামান্য অংশ যে প্রকাশ করতে পারে সেটা বিস্ময়কর : শুধুমাত্র প্রথাগত উপাদানের দ্বারাই নয়, বোধেন্দ্রিয়ের নির্বাচনীবৃত্তির দ্বারাও (selectiveness) আমাদের জ্ঞান সীমিত।
বোধেন্দ্রিয়ের নির্বাচনী বৃত্তির ফলে উদ্ভূত আমাদের সীমিত জ্ঞানের একটি উদাহরণ : শক্তির অবিনশ্বরতা। এ তথ্য পরীক্ষার সাহায্যে ক্রমান্বয়ে আবিষ্কৃত হয়েছে। মনে হয়েছিল এটা দৃঢ়ভিত্তিক পরীক্ষালব্ধ প্রাকৃতিক বিধি। এখন দেখা যাচ্ছে টী গাণিতিক অভিব্যক্তি গঠন করতে পারি যার গুণে এটা হবে দৃশ্যত অবিনশ্বর। তাহলে শক্তি অবিনশ্বর এই প্রস্তাব পদার্থবিদ্যার প্রতিজ্ঞারূপে (proposition) আর থাকে না– হয়ে দাঁড়ায় ভাষাতত্ত্ব আর মনস্তত্ত্বের প্রতিজ্ঞা। ভাষাতত্ত্বের প্রস্তাব অনুসারে : শক্তি আলোচ্য গাণিতিক অভিব্যক্তির নাম। মনস্তত্ত্বের প্রস্তাবরূপে : আমাদের বোধেন্দ্রিয় এমন যে আমরা আলোচ্য গাণিতিক অভিব্যক্তিটি মোটামুটি লক্ষ্য করি এবং আমাদের অমার্জিত বোধকে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ দ্বারা সংস্কার করতে করতে ক্রমশ ঐ গাণিতিক অভিব্যক্তির নিকটতর হই। পদার্থবিদরা শক্তি বিষয়ে নিজেদের জ্ঞান সম্পর্কে যা মনে করতেন এটা তার চাইতে অনেক কম।
পাঠক বলতে পারেন : পদার্থবিদ্যার তাহলে বাকি রইল কি? পদার্থময় জগৎ (world of matter) সম্পর্কে আসলে আমরা কি জানি? এক্ষেত্রে আমরা পদার্থবিদ্যার তিনটি বিভাগকে পৃথক করতে পারি। প্রথমত, সম্ভাব্য বিস্তৃতম সাধারণীকৃত অপেক্ষবাদের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি, দ্বিতীয়ত, যে বিষয়গুলিকে অপেক্ষবাদের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। তৃতীয়ত রয়েছে সেইগুলি, যেগুলিকে ভূগোল বলা চলে। এগুলিকে পরপর বিচার করা যাক।
প্রচলিত রীতি বাদ দিলে, অপেক্ষবাদ আমাদের বলে মহাবিশ্বের ঘটনাগুলির একটি চারমাত্রিক ক্রম (order) আছে এবং এই ক্রমে পরস্পর নিকটবর্তী হলে যে কোনো দুটি ঘটনার ভিতরে একটি সম্পর্ক রয়েছে, তার নাম অন্তর’ (interval)। উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন করলে এই অন্তর মাপা সম্ভব। অপেক্ষবাদ আরো বলে ‘পরম গতি’ (absolute motion), ‘পরম স্থান’ (absolute space) এবং ‘পরম কালের’ (absolute time) কোনো ভৌত গুরুত্ব থাকতে পারে না। এই সমস্ত কল্পনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পদার্থবিদ্যার বিধিগুলি গ্রহণযোগ্য নয়। এগুলি স্বতত ঠিক কোনো ভৌত বিধি নয় বরং এগুলি কিছু প্রস্তাবিত ভৌত বিধিকে সন্তোষজনক নয় এই কারণে পরিত্যাগ করার সামর্থ্য আমাদের দান করার জন্য একটি প্রয়োজনীয় নিয়ম।
ভৌতবিধিরূপে পরিচিত হওয়ার মতো এছাড়া যা অপেক্ষবাদে রয়েছে তা অতি সামান্য। তাছাড়া গণিত রয়েছে প্রচুর। তাতে দেখানো হয়েছে গাণিতিকভাবে গঠিত কিছু রাশিকে অবশ্যই আমাদের অনুভূত বস্তুর মতো আচরণ করতে হবে এবং রয়েছে পদার্থবিদ্যা এবং মনস্তত্ত্বের ভিতরে একটি সেতুর ইঙ্গিত। সে ইঙ্গিত হল : আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় যা বোধ করবার জন্য অভিযোজিত সেগুলি এবং গাণিতিকভাবে গঠিত এই রাশিগুলি অভিন্ন। কিন্তু কঠোরভাবে বিচার করলে এর কোনোটিই পদার্থবিদ্যা নয়।
পদার্থবিদ্যার যে অংশ বর্তমানে অপেক্ষবাদের আওতায় আনা যায় না সে অংশ বৃহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ। অপেক্ষবাদে এমন কিছু নেই যা দেখাতে পারে কেন ইলেকট্রন আর প্রোটন থাকবে। পদার্থের কেন ক্ষুদ্র পিণ্ডরূপ অস্তিত্ব থাকবে সে সম্পর্কেও কোনো যুক্তি অপেক্ষবাদ দেখাতে পারে না। এ অঞ্চল কোয়ান্টাম তত্ত্বের অধিকারে এ তত্ত্ব ক্ষুদ্র অবস্থাগত পদার্থের বহুধর্মের কারণ দেখাতে পারে। কোয়ান্টাম তত্ত্বের সঙ্গে বিশিষ্ট অপেক্ষবাদের সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে কোয়ান্টাম তত্ত্বের সঙ্গে ব্যাপক অপেক্ষবাদের সংশ্লেষণের (synthe sis) সমস্ত চেষ্টা। পদার্থবিদ্যার এই অংশকে ব্যাপক অপেক্ষবাদের কাঠামোর ভিতরে নিয়ে আসার ব্যাপারে অত্যন্ত কঠিন কিছু সমস্যা রয়েছে, কোয়ান্টাম তত্ত্বের নিজের ভিতরেও রয়েছে একই রকম কঠিন সমস্যা এবং অনেক পদার্থবিদের ধারণা কোয়ান্টাম তত্ত্ব এবং ব্যাপক অপেক্ষবাদের সংশ্লেষণ (syn thesis) হয়তো এই সমস্যাগুলির ভিতরে কয়েকটির সমাধান করতে পারবে। আমরা দেখেছি এখানকার পরিস্থিতি হল : অতি বৃহৎ মানে (matter on a very large scale) পদার্থের ধর্ম সম্পর্কে ব্যাপক অপেক্ষবাদ বেশ সন্তোষজনক বিবরণ (accounts? কারণ) দান করে, আর কোয়ান্টাম তত্ত্ব দান করে অতি ক্ষুদ্র মানের পদার্থের ধর্ম সম্পর্কে বেশ সন্তোষজনক বিবরণ। দুটি তত্ত্বের ভিত্তিতে কিছু ঐক্য রয়েছে কিন্তু এ দুটিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য যে গবেষণা করা হয়েছে এখনো সেগুলিকে দূরে কল্পনাভিত্তিক (speculative) রূপেই বিচার করা উচিত। অনেকে মনে করেন ব্যাপক অপেক্ষবাদকে এমনভাবে বিস্তৃত করা সম্ভব যে, কোয়ান্টাম তত্ত্ব যে সমস্ত ফল (result) ব্যাখ্যা করে সেগুলিও ব্যাখ্যাত হবে এবং সে ব্যাখ্যা হবে বর্তমান কোয়ান্টাম তত্ত্বেরও ব্যাখ্যার চাইতে অনেক বেশি সন্তোষজনক। এই চিন্তাধারা যাদের ছিল, মৃত্যুর আগে আইনস্টাইনও ছিলেন তাদের একজন। বর্তমানের বহু পদার্থবিদ্যাবিদই কিন্তু ভাবেন এ দৃষ্টিভঙ্গি ভ্রান্ত।
ব্যাপক অপেক্ষবাদ পারস্পরিক (next-to-next) পদ্ধতির চরম উদাহরণ। মহাকর্ষের কারণ গ্রহের উপর সূর্যের ক্রিয়া, একথা ভাববার আর প্রয়োজন নেই, বরং ভাবা যায় গ্রহটি যে অঞ্চলে রয়েছে মহাকর্ষ সেখানকার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের অভিব্যক্তি। অনুমান করা হয় স্থান-কালের এক অংশ থেকে অন্য অংশে যাওয়ার সময় এই বৈশিষ্ট্যগুলির পরিবর্তন হয় অল্পে অল্পে, ক্রমান্বয়ে (gradually), অবিচ্ছিন্নভাবে–সহসা উল্লম্ফনের (sudden jumps) সাহায্যে নয়। বিদ্যুৎচুম্বকত্বের ক্ষেত্রে ক্রিয়াগুলিকেও এইভাবে বিচার করা যায় কিন্তু বিদ্যুৎচুম্বকত্বের সঙ্গে যখনই কোয়ান্টাম তত্ত্বের সামঞ্জস্য বিধান করা যায় তখনই হয় এর চরিত্রের আমূল পরিবর্তন। অবিচ্ছিন্ন অবয়ব (continuous aspect) অদৃশ্য হয় এবং তার স্থলে প্রতিস্থাপিত হয় বিচ্ছিন্ন আচরণ (discontinuous behaviour)। আগেই আমরা দেখেছি এটাই কোয়ান্টাম তত্ত্বের জাতিরূপ (typ ical)। কিন্তু কোয়ান্টাম তত্ত্বের এই ধারণাগুলিকে যদি আমরা মহাকর্ষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চাই তাহলে আমরা দেখতে পাব এ দুটি ঠিক মতো খাপ খায় না এবং দুটি তত্ত্বের যে কোনো একটির কিংবা দুটি তত্ত্বেরই যথেষ্ট পরিবর্তন প্রয়োজন। কি পরিবর্তন প্রয়োজন সেটা এখনো জানা যায়নি।
এ সঙ্কটকে একটু অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী যখন সূর্যকে পর্যবেক্ষণ করেন পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষ সূর্যের ঔদাসীন্য তখন রাজকীয়। কিন্তু একজন পদার্থবিজ্ঞানী যখন অনুসন্ধান করতে চেষ্টা করেন একটা পরমাণুতে কি ঘটছে, তখনকার ব্যবহৃত যন্ত্রটি যা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে তার চাইতে অনেক ছোট না হয়ে বরং অনেক বড়। সুতরাং যন্ত্রটির পরমাণুর উপর ক্রিয়া থাকার সম্ভাবনা। দেখা গিয়েছে একটি পরমাণুর অবস্থান নির্ণয়ের জন্য যে ধরনের যন্ত্র সবচাইতে উপযুক্ত, সে যন্ত্র পরমাণুর বেগকে প্রভাবিত করতে বাধ্য এবং বেগ নির্ণয়ের জন্য যে যন্ত্র সবচাইতে উপযুক্ত সে যন্ত্র পরমাণুর অবস্থান প্রভাবিত করতে বাধ্য। পারমাণবিক কোয়ান্টাম তত্ত্ব এবং বিশিষ্ট অপেক্ষবাদের সমন্বয় করলে এ অসুবিধাগুলি হয় না। কারণ তখন মহাকর্ষকে অগ্রাহ্য করা হয় এবং কাছাকাছি পরমাণু থাকুক কিংবা না থাকুক স্থান-কালকে ভাবা হয় সমতল (flat)। কিন্তু আমরা যখন কোয়ান্টাম তত্ত্ব এবং ব্যাপক অপেক্ষবাদের সমম্বয় সাধন করতে চেষ্টা করি মহাকর্ষকে তখন অগ্রাহ্য করা হয় না সুতরাং স্থান-কালের বক্রতা নির্ভর করবে পরমাণুর অবস্থিতির উপর। এইমাত্র কিন্তু আমরা দেখেছি কোয়ান্টাম তত্ত্ব স্পষ্টভাবে বলে পরমাণুর অবস্থান কোথায় সেটা আমরা সব সময় জানতে পারি না। সঙ্কটের একটা উৎস এখানে।
শেষে আমরা আসি ভূগোলের প্রসঙ্গে। এর ভিতরে আমরা ইতিহাসকেও অন্তর্ভুক্ত করেছি। ইতিহাসের সঙ্গে ভূগোলের বিচ্ছিন্নতার ভিত্তি, স্থানের সঙ্গে কালের বিচ্ছিন্নতা। যখন আমরা স্থান-কালে এই দুটিকে একত্রিত করি তখন আমাদের প্রয়োজন হয় ইতিহাস ভূগোলের সমন্বয়ের জন্যও এতটি শব্দ। সারল্যের খাতিরে, বিস্তৃত অর্থে আমি একটি শব্দ ভূগোলেই ব্যবহার করব।
স্থান-কালের এক অংশ থেকে অন্য অংশের পার্থক্য নির্ণয় করে এরকম অসংস্কৃত বাস্তব তথ্য যত কিছু আছে, এ অর্থে তার সবটাই ভূগোলের অন্তর্ভুক্ত। এক অংশ সূর্যের অধিকারে, এক অংশ পৃথিবীর, মধ্যবর্তী অঞ্চলে রয়েছে আলোকতরঙ্গ, কিন্তু কোনো পদার্থ নেই (এখানে ওখানে সামান্য পরিমাণ ছাড়া)। বিভিন্ন বাস্তব ভৌগোলিক ঘটনার ভিতরে কিছু পরিমাণ তাত্ত্বিক সম্পর্ক রয়েছে। ভৌত বিধির উদ্দেশ্য এ সম্পর্ককে প্রতিষ্ঠিত করা।
এখনই আমরা সৌরতন্ত্রের অতীতে আর ভবিষ্যতে ব্যাপ্ত বিশাল কালের বৃহৎ ঘটনাগুলির গণনা করতে সক্ষম। কিন্তু এই জাতীয় সমস্ত গণনার জন্য আমাদের অসংস্কৃত বাস্তব ঘটনার ভিত্তি প্রয়োজন। বাস্তব ঘটনাগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু বাস্তব ঘটনাগুলির অনুমিতি (inference) একমাত্র অন্য বাস্তব ঘটনা থেকেই সম্ভব, শুধু সাধারণ বিধি থেকে নয়। সুতরাং পদার্থবিদ্যায় ভৌগোলিক বাস্তব ঘটনাবলীর একটি অন্য নিরপেক্ষ স্থান রয়েছে; যদি আমাদের অনুমতির জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্ত হিসাবে অন্য বাস্তব ঘটনা আমরা না জানি তাহলে ভৌত বিধি যতই থাকুক না কেন ভৌত ঘটনা অনুমানের সামর্থ্য আমাদের হবে না। এ ক্ষেত্রে যখন আমি বাস্তব ঘটনাবলীর কথা বলছি তখন আমি ভাবছি ভূগোলের কয়েকটি বিশিষ্ট বাস্তব ঘটনার কথা। ভূগোল শব্দ আমি যে বিস্তৃত অর্থে ব্যবহার করছি এখানে সেই অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হল।
অপেক্ষবাদে আমাদের রিচার্য অবয়ব (structure) কিন্তু যে পদার্থ দিয়ে অবয়ব গঠিত সেটা বিচার্য নয়। অন্যদিকে ভূগোলে ঐ পদার্থ প্রাসঙ্গিক। একটি স্থানের (place) সঙ্গে অন্য একটি স্থানের যদি পাৰ্তক্য থাকতে হয় তাহলে হয় একটি স্থানের পদার্থের সঙ্গে অন্য স্থানের পদার্থের পার্থক্য থাকবে কিংবা কোনো স্থানে পদার্থ থাকবে এবং কোনো স্থানে থাকবে না। এই দুটি বিকল্পের ভিতরে প্রথমটিকেই বেশি সন্তোষজনক মনে হয়। আমরা বলতে চেষ্টা করতে পারি; ইলেকট্রন, প্রোটন এবং অন্যান্য উনপারমাণবিক কণা (sub-atomic particles) রয়েছে–বাকিটা শূন্য। কিন্তু শূন্য অঞ্চলে আলোকতরঙ্গ রয়েছে সুতরাং সেখানে কিছু নেই একথা আমরা বলতে পারি না। কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে, এমন কি বস্তুগুলি কোথায় আছে সে কথাও আমরা নির্ভুলভাবে বলতে পারি না। শুধুমাত্র বলতে পারি–একটি স্থানের তুলনায় অন্য একটি স্থানে ইলেকট্রন পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কারও কারও মতে আলোকতরঙ্গ এবং কণিকাগুলি ইথারের বিক্ষোভ মাত্র, অন্যরা শুধুমাত্র বিক্ষোভ বলেই খুশি। কিন্তু সে যাই হোক, যেখানেই আলোকতরঙ্গ কিংবা কণিকা থাকবার সম্ভাবনা রয়েছে, সেখানেই ঘটনা ঘটছে। যেখানেই কোনো রূপে মুক্তি থাকার সম্ভাবনা সে স্থান সম্পর্কে আমাদের বলার ক্ষমতা এই পর্যন্ত, তার কারণ শক্তি এখন একাধিক ঘটনার ভিত্তিতে গঠিত গাণিতিক গঠনের রূপ নিয়েছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি স্থান-কালের ঘটনা সর্বত্র রয়েছে কিন্তু যে অঞ্চল নিয়ে আমরা বিচার করছি সে অঞ্চলে একটি ইলেকট্রন কিংবা প্রোটন থাকবার খুব বেশি সম্ভাবনা আছে, না সে অঞ্চল সাধারণত আমরা যাকে শূন্যস্থান বলি সেরকম ঘটনাগুলির পার্থক্য হবে সেই অনুসারে। কিন্তু শুধুমাত্র যে ঘটনাগুলি নিজেদের জীবনকালের ভিতর সংঘটিত হয় সেই ঘটনাগুলি ছাড়া অন্যগুলির স্বকীয় চরিত্র (intrinsic nature) আমরা কিছুই জানতে পারি না। যে অসংস্কৃত ঘটনাগুলিকে পদার্থবিদ্যা একটি ছকে সাজায় আমাদের অনুভূতি এবং বোধ নিশ্চয়ই তার একটি অংশ কিংবা বলা যেতে পারে পদার্থবিদ্যা সেগুলিকে একটি ছকে সাজানো অবস্থায় আবিষ্কার করে। যে ঘটনাগুলি আমাদের জীবনের অংশ নয়, সেগুলির ছক পদার্থবিদ্যা আমাদের কাছে প্রকাশ করে কিন্তু ঘটনাগুলি স্বতত (in themselves) কি রকম সে কথা প্রকাশ করতে পদার্থবিদ্যা একেবারেই অক্ষম। অন্য কোনো পদ্ধতিতে এগুলি আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না।