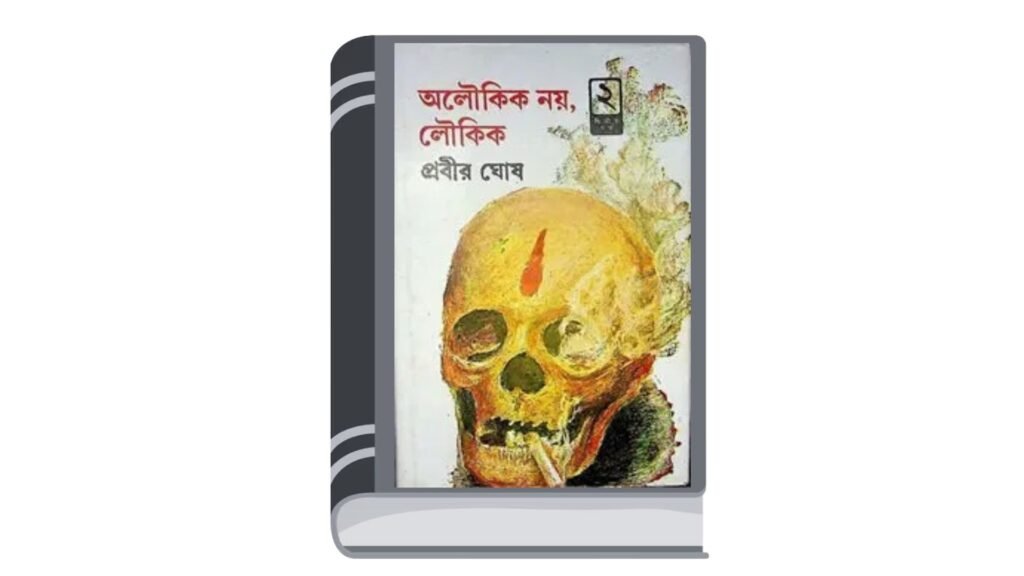অধ্যায় নয়: অবাক মেয়ে মৌসুমী’র মধ্যে সরস্বতীর অধিষ্ঠান (?) ও প্রডিজি প্রসঙ্গ
অবাক মেয়ে মৌসুমী’র মধ্যে সরস্বতীর অধিষ্ঠান (?) ও প্রডিজি প্রসঙ্গ
মৌসুমী প্রসঙ্গে গণমাধ্যম
১৯৮৯-এ রকেট গতিতে প্রচারের ব্যাপকতা পেয়ে দেশ-বিদেশ কাঁপিয়ে দিয়েছিল পশ্চিমবাংলার রুক্ষ জেলা পুরুলিয়ার এক সাত বছরের বালিকা মৌসুমী। অবাক মেয়ে মৌসুমী যে ‘Prodigy’ অর্থাৎ ‘পরম বিস্ময়কর প্রতিভা’, এই বিষয়ে প্রচার মাধ্যমগুলো সহমত পোষণ করলেও, কত বড় মাপের ‘প্রডিজি’ এটা প্রমাণ করতে দস্তুরমতো প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। কেন, যে পত্র-পত্রিকা বা প্রচার মাধ্যম মৌসুমীকে যত বড় প্রডিজি বলে প্রমাণ হাজির করতে পারবে, তার তত সুনাম, সম্মান ও বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধি পাবে। সেই সময় মৌসুমী সম্বন্ধে প্রচার মাধ্যমগুলোর বক্তব্য কী ধরনের ছিল সেটা বোঝাতে বহু থেকে গুটিকয়েক উদাহরণ এখানে হাজির করছি।
১৩ আগস্ট ’৮৯-এ আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রতিবেদক বিমল বসুর প্রতিবেদন প্রকাশিত হল ‘বুদ্ধিতে যে প্রতিভার ব্যাখ্যা নেই’ শিরোনামে। প্রতিবেদক বিজ্ঞান-লেখক হিসেবে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট পরিচিত। সাতটি ছবিসহ প্রচুর গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত প্রতিবেদনটির শুরুতেই বড় বড় হরফে লেখা ছিল, ‘অল্প বয়সে অসামান্য বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে সম্প্রতি হইচই ফেলে দিয়েছে পুরুলিয়ার মৌসুমী।’ লেখাটিতে শ্রীবসুর স্পষ্ট ঘোষণা—‘মৌসুমী এক বিস্ময়কর বালিকা। এককথায় প্রডিজি। এখন তার বয়স ঠিক সাত। কিন্তু ইতিমধ্যেই বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি—এই তিনটি ভাষায় যেমন বিস্ময়কর তার দক্ষতা, তেমনি পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত ইত্যাদি বিষয়েও সে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে।’
ওই প্রতিবেদনেই বলা হয়েছে, ‘কলকাতা পাভলভ ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা ডি এন গাঙ্গুলী বিস্ময় বালিকা মৌসুমী সম্পর্কে কিছু খোঁজখবর রাখেন। তাঁর এক ছাত্রকে পাঠিয়েও ছিলেন আদ্রায় মৌসুমীর সঙ্গে কথা বলতে। শ্রীগাঙ্গুলীর মতে, মৌসুমীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তির পিছনে আছে সম্ভবত বহু প্রজন্ম পূর্বের কোনও সুপ্ত জিন, এই মেয়েটির মধ্যে যার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।’
প্রতিবেদনটিতে ডি এন গাঙ্গুলীর মতামত হিসেবে আরও প্রকাশিত হয়েছে, ‘মৌসুমীর বুদ্ধির যে স্তর তাতে তার জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা চাই। বিদেশে বিশেষত আমেরিকার উচ্চবুদ্ধির ছেলেমেয়েদের বাছাই করে তাদের জন্য বিশেষ ধরনের পাঠক্রম ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।’
প্রতিবেদনটিতে প্রতিবেদক জানান, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগের প্রাক্তন প্রধান এবং মস্তিষ্কবিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডঃ জে জে ঘোষ আক্ষেপ প্রকাশ করে জানান, ‘মৌসুমীর মতো প্রডিজির সন্ধান পাওয়া সত্ত্বেও এখানকার বিজ্ঞানীরা ওকে নিয়ে তেমন মাথা থামাচ্ছেন না, সিরিয়াস গবেষণার কণা ভাবছেন না।’
জনপ্রিয় পাক্ষিক ‘সানন্দা’র ৭ সেপ্টেম্বর ’৮৯ সংখ্যায় মৌসুমীকে নিয়ে একটি প্রচ্ছদ কহিনি ‘বিশেষ রচনা’ প্রকাশিত হয়। শিরোনামে ছিল ‘অবাক পৃথিবীর অবাক মেয়ে’। আটটি রঙিন ছবিতে সাজানো এই বিশেষ রচনার রচয়িতা সুজন চন্দ মৌসুমীর ইংরেজি উচ্চারণ প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন, ‘একেবারে মেম সাহেবের মতো উচ্চারণ।’ শ্রীচন্দ আরও জানাচ্ছেন, ‘সেই তুলনায় বাংলা উচ্চারণ ততটা ভালো নয়। কিছুটা আঞ্চলিক টান আছে তাতে। তবে হিন্দি উচ্চারণে বেশ মুন্সিয়ানা আছে।”
মৌসুমীর টাইপের স্পিড সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শ্রীচন্দ জানাচ্ছেন, ‘ও যেভাবে দ্রুত টাইপ করছিল তাতে হলফ করেই বলা যায় স্পিড কম করেও ৪৫। চমৎকার ফিঙ্গারিং।’
প্রতিবেদক আরও জানিয়েছেন, শুধু জ্ঞানের পরীক্ষা নয়, বুদ্ধির ও রাজনীতির পরীক্ষাতেও মৌসুমী পাকা ডিপ্লোম্যাট। মৌসুমী এখন গবেষণা করছে কয়লাকে সালফারমুক্ত করা নিয়ে। এ কাজে সফল হলে বায়ুদূষণ থেকে যুক্ত হবে পৃথিবী। মৌসুমীর ধারণা ও সফল হবেই, নোবেল প্রাইজ পাবে এর সাড়ে ন-বছর বয়সের মধ্যেই।
জনপ্রিয় বাংলা মাসিক ‘আলোকপাত’ মৌসুমীকে নিয়ে প্রচ্ছদকহিনী প্রকাশ করে সেপ্টেম্বর ৮৯ সংখ্যায়। শিরোনাম—‘বিস্ময় বালিকা মৌসুমী: সাত বছরের সরস্বতী’, সঙ্গে ছিল আধ ডজন ছবি। প্রতিবেদনটির শুরুতেই বড় বড় হরফে লেখা ছিল—
শিরোনামে মৌসুমীকে কেন সরস্বতী বলা হয়েছে, তারই উত্তর মেলে মৌসুমীর মা শিপ্রাদেবীর কথায়। প্রতিবেদকের ভাষায়, ‘শিপ্রাদেবী জানান, মৌসুমীর জন্মের আগে এক আশ্চর্য অনুভূতি মাঝে মধ্যে গ্রাস করে ফেলত শিপ্রাদেবীকে। শিপ্রাদেবী তা স্বামীকেও বলতেন। মাতৃগর্ভে মৌসুমীর আসার আগে শিপ্রাদেবী এক রাত্রে স্বপ্ন দেখেন তাঁর আরাধ্য দেবী লক্ষ্মী শ্বেতবর্ণা রূপ নিয়ে অনেক দূরের থেকে হেঁটে আসছেন তাঁর দিকে। স্বপ্নের মধ্যেই তিনি দেখলেন কোলের কাছে আসামাত্রই অদৃশ্য হয়ে গেলেন।’
“আদ্রা রেলশহরের ৭ বছরের
মৌসুমী চক্রবর্তী বাংলা, হিন্দী,
ইংরাজি ভাষায় সারা বিশ্বের রাজনীতি,
সমাজনীতি, অর্থনীতি, অধ্যাত্মবাদ এবং বিজ্ঞান
বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে এবং পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা
পর্ষদ থেকে ৯ বছর বয়সে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসবার
অনুমতি পেয়ে ‘বিস্ময় বালিকা’ হিসেবে নিজেকে
প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিস্ময়বালা মৌসুমীর
এই জীবন কাহিনী পেশ করা হল তার সঙ্গে
দুদিনব্যাপী দীর্ঘ ১৮ ঘণ্টা ধরে নেওয়া
ইন্টারভিউ-এর প্রেক্ষাপটে।”
শিপ্রাদেবীর এই স্বপ্নের কথা পাঠকরা ‘খেয়েছিলেন’ ভালো, যুক্তিটা তাঁদের অনেকেরই মনে ধরেছিল—স্বয়ং সরস্বতী ভর না করলে এমন বিদ্যে বুদ্ধি কি এই বয়সে হওয়া সম্ভব?
প্রতিবেদক আরও জানিয়েছেন, ‘মৌসুমীর সঙ্গে বর্তমান প্রতিবেদক দু-দফায় প্রায় ১৮ ঘণ্টা সাক্ষাৎকার করেন। সেই সাক্ষাৎকারে সাহিত্য, সংস্কৃতি, সিনেমা, রাজনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, চিত্রকলা, অধ্যাত্মবাদ কিছুই বাদ ছিল না। আর প্রতিটি আলোচনাতেই মৌসুমী এই প্রতিবেদকের জ্ঞানের সীমারেখা থেকে অনেক উঁচুতে থেকে সব উত্তর দিয়েছেন।’ ….“সাত বছরের মৌসুমী টাইপেও সিদ্ধহস্ত। ওর সমস্ত রিসার্চ পেপার ও নিজেই টাইপ করে। টাইপে ওর স্পিড ইংরাজিতে ৯০ এবং বাংলায় ৪০। মৌসুমী খুব ভালো গানও গাইতে পারে। রবীন্দ্রসঙ্গীত, রাগপ্রধান দুধরনেরই।”
আরও বহু পত্র-পত্রিকার মতো এই পত্রিকাতেও ঘুরেফিরে মৌসুমীর রিসার্চের কথা এসেছিল। প্রতিবেদক জানাচ্ছেন, মৌসুমীর বাবা ‘সাধনবাবুর ব্যবহার খুবই আন্তরিক। আমাদের জন্য চা পর্বের ব্যবস্থা করে এসে জানালেন—মৌসুমী একটু রিসার্চের কাজ করছে। আধঘণ্টা পরেই আসছে। রিসার্ট? চমকে উঠলাম, সাত বছরের মেয়ে রিসার্চ করছে-সে আবার কি? মনের ভাব গোপন রেখে বললাম,—রিসার্চ? আপনার মেয়ে রিসার্চ করে নাকি?
—হ্যাঁ, তবে বিষয়টা বলতে পারব না। শুধু এটুকু বলতে পারি, যে বিষয়টা নিয়ে রিসার্চ করছে সেটা অবশ্যই মানব কল্যাণের পক্ষে।
—মৌসুমী বহুবারই বলেছে সে ডাক্তার হতে ভালোবাসে। তা এই রিসার্চ চিকিৎসা বিজ্ঞানের কোন কাজে লাগবে?
—বললাম তো, এর রিসার্চ সফল হলে ভারতের মর্যাদা বিশ্বের দরবারে বেড়ে যাবে। আর এই রিসার্চ এত গোপনীয় রাখার কারণ হল, বিষয়টি এতই নতুন এবং প্রয়োজনীয় যে খবর বাইরে গেলে আমরা বিপদে পড়ে যেতে পারি।”
—আচ্ছা, এর আগে মৌসুমী কি কোন বিষয়ের উপর রিসার্চ করেছে?
—কয়লার ওপর কাজও করেছে। তবে সেটা উল্লেখ করার মতো নয়। আর সে ব্যাপারটায় ওকে এগোতে দিইনি। এই বড় কাজটির দিকে তাকিয়ে। আসানসোল বি ই কলেজের অধ্যাপকরা ওকে নিয়ে এখানে একবার একটা গ্রুপ ডিসকাশন করেছিলেন।’
মৌসুমী রিসার্চ করছে। অর্থাৎ ওর জ্ঞান বিজ্ঞানে মাস্টার ডিগ্রির সীমাকে অতিক্রম করেছে এবং ও আর আড়াই বছরের মধ্যে বিজ্ঞান নোবেল পুরস্কার পাবে এই বিশ্বাস বহু বঙ্গবাসী ও ভারতবাসীকে প্রাণীত করেছিল, গর্বিত করেছিল।
৩০ জুলাই ১৯৮৯। দিল্লি দূরদর্শনের রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের ইংরেজি সংবাদে প্রায় দুমিনিট ধরে নানাভাবে মৌসুমীকে হাজির করা হল কোটি কোটি দর্শকদের কাছে। মানুষ দেখলেন, পরিচিত হলেন ‘ওয়াণ্ডার গার্ল’-এর বিস্ময়কর প্রতিভার সঙ্গে।
এরও দু-বছর আগে আমরা একটু পিছিয়ে গেলে মন্দ হয় না। ‘দ্য স্টেটসম্যান’ দৈনিক পত্রিকা ২১ এপ্রিল ’৮৭ মৌসুমীর এক বিশাল ছবি-সহ দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল, ‘Wonder girl of Purulia Village’। প্রতিবেদক অলোকেশ সেন। তখন মৌসুমীর বয়স মাত্র চার বছর আট মাস।
প্রতিবেদক মৌসুমীর প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন, “Mousumi’s interest on studies became evident when she was only one and a half years old. Since then she has learnt to read, write and speak in Bengali, Hindi and English. At present, she is learning German at home.”
অর্থাৎ, মৌসুমীর পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ সূচিত হয় মাত্র দেড় বছর বয়সে। তারপর ও বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজিতে পড়তে, লিখতে ও বলতে শিখেছে। বর্তমানে বাড়িতেই জার্মান শিখছে।
প্রকাশিত ছবিতে দেখা যাচ্ছে মৌসুমী টাইপ করছে। ছবির তলায় লেখা—Mousumi Chakraborty typing out some paragraph from one of her text books.
সমাজ সচেতন বিজ্ঞানমনস্ক বলে স্ববিজ্ঞাপিত মাসিক পত্রিকা ‘উৎস মানুষ’ আগস্ট ’৮৭ সংখ্যায় মৌসুমীকে নিয়ে প্রচ্ছদকাহিনি করলেন, ছবি-সহ। শিরোনাম ছিল, ‘পুরুলিয়ার আশ্চর্য মেয়ে মৌসুমী।’ প্রতিবেদক অভিজিৎ মজুমদার।
পাঠকরা একটু লক্ষ্য করতেই দেখতে পাবেন, প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হবার সময়ও মৌসুমী পাঁচের কোঠায় পা দেয়নি। প্রতিবেদক অবশ্য জানাচ্ছেন সাড়ে চার বছরের মৌসুমীকে ধানবাদের সেণ্ট্রাল ফুয়েল রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর বিজ্ঞানীরা ‘অজস্র প্রশ্ন করেছে ইংরেজি, বাংলা বা হিন্দিতে। যেমন সালফিউরিক বা নাইট্রিক অ্যাসিডের সংকেতিক নাম কিংবা কয়লা গবেষণা বিষয়ে নানা জটিল উত্তর দিয়ে সবাইকে অবাক করেছে।’ সেই সঙ্গে প্রতিবেদক এও জানিয়েছেন, এত সব উত্তর দিচ্ছে—‘যদিও সব কথা এখনো স্পষ্ট নয়।’ সত্যিই তো সাড়ে চার বছর আধো-আধো কথা বলারই বয়স।
উৎস মানুষ আরো জানাচ্ছে, ‘বিস্ময়ের ব্যাপার, মৌসুমী টাইপ মেসিনে অনায়াসে টাইপ করতে পারে নির্ভুল ফিংগারিং-এ প্রায় চল্লিশ স্পিড-এ।’ …‘এই শেষ নয়। মৌসুমী জানে বাংলা ব্যাকরণ, ভৌতবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞানের নানা কথা। অঙ্কের অনেক ফরমুলাই ওর ঠোটের ডগায়। অনুবাদ করতে পারে বাংলা, ইংরাজি বা হিন্দিতে। সম্প্রতি ও জার্মান ভাষা শিখছে।’…‘মৌসুমীর মাও খুব ভালো ছাত্রী ছিলেন।’ আর মৌসুমীর বাবা? প্রচার মাধ্যমগুলোর কল্যাণে তাও কারোই অজানা ছিল না। তিনি ছিলেন জুনিয়র সায়েনটিস্ট।
মৌসুমীকে নিয়ে গণ-উন্মাদনার মতোই এক ধরনের প্রচার-উন্মাদনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। এবং তা প্রভাবিত করেছিল বিভিন্ন পেশার মানুষকে! ফলশ্রুতিতে আমি এবং আমাদের সমিতি প্রচুর চিঠি পেয়েছি। চিঠিগুলো এসেছিল মৌসুমীর বিষয়ে বিভিন্ন রকমের কৌতূহল নিয়ে, দ্বন্দ্ব নিয়ে, বিভ্রান্তি নিয়ে, জিজ্ঞাসা নিয়ে। তখন থেকে আজ পর্যন্ত অগুনতি সেমিনারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মৌসুমীকে নিয়ে হাজারো প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েই চলেছি। প্রশ্নগুলো মোটামুটি এই জাতীয়—মৌসুমীর এই পরম বিস্ময়কর প্রতিভার ব্যাখ্যা কী? বাস্তবিকই কি মৌসুমী পরম বিস্ময়কর প্রতিভা? মৌসুমী কি তবে জাতিস্মর? অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারিণী? ও কি মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ বলতে সক্ষম? এর মধ্যে বাস্তবিকই কি ঈশ্বরের প্রকাশ ঘটেছে? মা লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে ঘিরে মৌসুমীর মা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, মৌসুমীর প্রতিভা কি সেই স্বপ্নেরই বাস্তবরূপ নেওয়ার প্রমাণ নয়? মৌসুমী কি লক্ষ্মী ও সরস্বতীরই অংশ? স্বয়ং সরস্বতী মৌসুমীর জিভের ডগায় না থাকলে মুখে ভালোমতো বুলি ফোটার আগেই কী করে গবেষণা করে, বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে পরীক্ষায় গুণিজনদের হতবাক করে দেয়?

এরই পাশাপাশি অন্য ধরনের প্রশ্নও এসেছে—মৌসুমী ’৯১-তে মাধ্যমিক দেবে, অর্থাৎ ওর বিদ্যে বুদ্ধি ক্লাস নাইনের মানের। অথচ অনেক পত্র-পত্রিকার প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে মৌসুমী গবেষণা করছে বিজ্ঞান নিয়ে। ওর বিদ্যে বুদ্ধি অনার্স গ্র্যাজুয়েট স্তরের। ইংরেজি টাইপের স্পিড কেউ বলছেন কম করে ৪৫, কেউ ৬০, কেউবা বলছেন ৯০। বাংলায় টাইপ করছে ৪০ স্পিডে। কখনও জানা যাচ্ছে মৌসুমী বিজ্ঞানী হতে ইচ্ছুক, কখনও জানা যাচ্ছে ডাক্তার হতে চায়। কোন প্রতিবেদক লিখলেন সাহিত্য, সংস্কৃতি, সিনেমা, রাজনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, চিত্রকলা, অধ্যাত্মবাদ নিয়ে প্রতিটি আলোচনাতেই মৌসুমী প্রতিবেদকের জ্ঞানের সীমারেখা থেকে অনেক উঁচুতে থেকে সব উত্তর দিয়েছে। কেউ জানাচ্ছেন, মৌসুমী তার সাড়ে ন-বছর বয়সেই গবেষণার ফসল হিসেবে আনবে নোবেল পুরস্কার। বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি তিনটি ভাষাতেই বিস্ময়কর তার দক্ষতা। জানে ডাচ, জর্মান। পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত সবেই ওর অগ্রগতি বিস্ময়কর। স্বভাবতই বহুজনের কাছেই বিরাট জিজ্ঞাসা—মৌসুমীর শিক্ষার প্রকৃত মান কী? আর এইসব জিজ্ঞাসারই মুখোমুখি হতে হয়েছে আমাকে বার বার এবং তা শুধু সেমিনারে নয়, বিয়েবাড়িতে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, অফিসে, সহযোগী বিজ্ঞানকর্মীদের কাছে, সাংবাদিক বন্ধুদের কাছে। একাধিক সংবাদপত্রের প্রতিনিধি এই বিষয়ে আমার মতামত জানতে চেয়েছেন। প্রত্যেকেই বিনীতভাবে জানিয়েছিলাম, “এখনও মৌসুমীকে দেখিনি, মৌসুমীর মুখোমুখি হইনি। তাই মৌসুমীর বিষয়ে কোনও কিছু মন্তব্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব।” জনৈক সাংবাদিক কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের নাম জানিয়ে বলেছেন, এঁরা প্রত্যেকেই মৌসুমীকে পরীক্ষা না করেই তো মতামত জানিয়েছেন। বলেছিলাম, “এঁরা আপনাদের বা নিজেদের বিশ্বাসযোগ্য কারও মাধ্যমে মৌসুমীর ওপর পরীক্ষা চালিয়ে মতামত জানাবার যে ক্ষমতা রাখেন, আমার সে ক্ষমতা নেই। এই অক্ষমতা বিনীতভাবে স্বীকার করে নিয়েই জানাচ্ছি—মৌসুমীকে নিজে পরীক্ষা না করে কোনও মন্তব্য করতে আমি অপারগ।”
প্রডিজি কী? ও কিছু বিস্ময়কর শিশু প্রতিভা
পরম বিস্ময়কর শিশু প্রতিভার অনেক কাহিনিই মাঝে-মধ্যে শোনা যায়। এদের বেশিরভাগই বিখ্যাত হয় মিথ্যা প্রচারে, গুজবে, অলীক কল্পনায়। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ঈশ্বরের কৃপাধন্য, ঈশ্বরের অংশ বা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা নেই—ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত হয়। বেশ কিছু শিশু প্রতিভার খবর অবশ্য নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে আমরা অভ্রান্ত বলে মেনে নিই। বাস্তবিকই যারা পরম বিস্ময়কর শিশু প্রতিভা তাদের ক্ষেত্রেও ‘বুদ্ধিতে যে প্রতিভার ব্যাখ্যা নেই’ ধরনের কোনও বিশেষণ প্রয়োগ একান্তই বিজ্ঞান বিরোধী, বিজ্ঞানমনস্কতা বিরোধী চিন্তার ফসল। একজন বিজ্ঞান বিষয়ক লেখার সঙ্গে যুক্ত মানুষ এই ধরনের বাক্য প্রয়োগ করলে যে কোনও যুক্তিবাদী মানুষকেই তা ব্যথিত করে, শঙ্কিত করে কারণ,—
বিজ্ঞান বর্তমানে যতটুকু এগোতে পেরেছে তারই সাহায্যে যে
কোনও অসাধারণ বিস্ময়কর প্রতিভাধরের কার্যকলাপের
ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে; তা সে শিশু মস্তিষ্কের
স্বাভাবিক শারীরভিত্তিক ধর্মের অকাল বিকাশের
ফলেই হোক, জেনেটিক কোনও
কারণেই হোক, অথবা অন্য
যে কোনও কারণেই
হোক।
সব দেশেই বিভিন্ন সময়ে বিস্ময়কর প্রতিভাধর শিশুর দেখা মেলে। এরা কেউ পড়াশুনোয়, কেউ খেলাধুলোয়, কেউ সঙ্গীতে, কেউ নৃত্যে, কেউ বা ছবি আঁকায় অথবা অন্য কোনও বিষয়ে বিরল প্রতিভা বলে চিহ্নিত হয়েছে। এদের অনেকেই পরবর্তীকালে চূড়ান্তভাবে নিজের প্রতিভাকে বিকশিত করতে সমর্থ হয়েছে, আবার অনেকে হারিয়ে গেছে সাধারণের মিছিলে।
আবার এর বিপরীতটাও ঘটতে দেখা গেছে বহুক্ষেত্রে। শৈশবে যার মধ্যে অসাধারণত্বের হদিশ খুঁজে পাওয়া যায়নি, পরবর্তী সময়ে তারই প্রতিভাকে মানুষ বার বার সেলাম জানিয়েছে। মাইক্রোস্কোপের আবিষ্কারক লিউয়েনহুক, বিবর্তনবাদের প্রবক্তা চার্লস ডারউইন, বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা শরৎচন্দ্র—এঁরা কেউই শিশু প্রডিজি ছিলেন না। বরং লিউয়েনহুক এবং ডারউইন ‘ফালতু’ বলেই চিহ্নিত হয়েছিলেন। লেখাপড়ায় মোটেই জুতসই ছিলেন না, ছিলেন নড়বড়ে। ছাত্র জীবনে আইনস্টাইনও এঁদের থেকে ভিন্নতর কিছু ছিলেন না। একবার পদার্থবিদ্যায় অকৃতকার্যও হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ছাত্রজীবনও কৃতিত্বপূর্ণ ছিল না, শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রেও একই কথাই বলতে হয়। বিশ্বত্রাস বোলার চন্দ্রশেখর শৈশবে পোলিও-তে আক্রান্ত হয়ে চিহ্নিত হয়েছিলেন ‘বিকলাঙ্গ’ হিসেবে। তাঁর ক্রীড়া-জগতে অক্ষয় কীর্তি স্থাপনের কথা সেই সময় কারো কষ্ট-কল্পনাতেও আসেনি। এমন উদাহরণ বহু আছে।
আমাদের দেশে শুধু মৌসুমীই নয়, বর্তমানে আরো কয়েকজনের সন্ধান পাওয়া গেছে, যারা বিস্ময়কর শিশু প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে। এমনই একজন চার বছরের মেয়ে পায়েল। ’৮৯-তে পুণে ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতায় ২ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট ৫২ সেকেণ্ডে দৌড় শেষ করে সারা বিশ্বকে চমকিত করেছে। দৌড়ের সময় পায়েলের ওজন ছিল মাত্র ১৫ কেজি, উচ্চতা ৫৪ মিটার। অনসূয়া নটরাজন ১১ বছরের বালিকা। নিবাস কলকাতায়। ভারতনাট্যমে অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে বহু গুণিজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ইতিমধ্যেই। ভাল ও লয়ের দখল, ভাব উপলব্ধির ক্ষমতা বিস্ময়কর।
মধ্যপ্রদেশের গ্রামের ছেলে ন-বছরের বীরেন্দ্র সিং ইতিমধ্যেই ৩০০ কবিতা লিখেছে, যেগুলো কাব্যগুণে সাহিত্যিক ও সাহিত্য-রসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ভোপালের কবি মহল থেকে পেয়েছে ‘বাল কবি নাদান’ উপাধি। ওর প্রতিভার প্রকাশ মাত্র চার বছর বয়সে। ওর কাব্য প্রতিভা শুধু কবিতাতেই আবদ্ধ থাকেনি। বেশ কিছু গল্পও লিখেছে, লিখেছে সিনেমার চিত্রনাট্য। ইতিমধ্যে বোম্বাই ফিল্ম জগতের চিত্র-পরিচালক শেখর কাপুরের ফিল্মে সাহায্যকারী হিসেবে নাকি থাকার আমন্ত্রণ পেয়েছে।
অমিত পাল সিং চাড্ডা ক্লাস থ্রির ছাত্র। পড়ে বালভারতী এয়ারফোর্স স্কুলে। ইতিমধ্যে জীবন্ত ‘ইয়ার বুক’ হিসেবে অনেক প্রচার মাধ্যমের নজর কেড়েছে। টু-তে পড়তে ওর বাবা কিনে দিয়েছিলেন ‘কম্পিটিশন সাকসেস রিভিউ’। মাত্র দু-ঘণ্টায় মুখস্থ করে অমিত শুরু করেছে ওর জয়যাত্রা।
আমেরিকার টেলিভিশন একটি সাত বছরের শিশুর অদ্ভুত কাণ্ডকারখানার সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছে কোটি কোটি দর্শকের। শিশুটি ভারতীয়—জিপসা মাক্কর। মারুতি, ফিয়াট ও মারুতি জিপসি ঘণ্টায় ৬০ থেকে ৮০ কিলোমিটার বেগের দূরত্ত-গতির স্টিয়ারিং কণ্ট্রোল করছে চূড়ান্ত নিখুঁতভাবে।
অন্ধ্রে কিশোর শ্রীনিবাস মাত্র ছ-বছর বয়সেই ম্যাণ্ডোলিন বাজানো শুরু করেছিল। বর্তমান বয়স ১৯। বিদেশি এই যন্ত্রে ভারতীয় রাগ-রাগিণীর সুর সাগরে দেশ বিদেশের সুর-রসিকদের ভাসিয়ে দিয়ে গেছে।
পেরামবুরের ন-বছরের বাসুদেবন মুখে মুখে চার অঙ্কের যে কোনও সংখ্যার স্কোয়ার রুট, কিউব রুট, ফোরথ রুট করে ফেলছে।
তেরো বছরের ভরতনাট্যম শিল্পী বর্ণনা বসু ভালে, লয়ে, ভাবে বিস্ময়কর শিশু প্রতিভার প্রমাণ রেখেছে।
ক্যালিফোর্নিয়ার প্রবাসী ভারতীয় ন’বছরের শ্বেতা ভরদ্বাজ আজ ভারতনাট্যমের পেশাদার নৃত্যশিল্পী। মুদ্রা, তাল, লয়, ভাবে এক কথায় অনন্য।
বাঙ্গালোরের ১৬ বছরের কিশোর আর নিরঞ্জন কম্পিউটার প্রয়োগে নতুন তত্ত্ব হাজির করে বিশ্বের কম্পিউটার বিশেষজ্ঞদের যথেষ্ট নাড়া দিয়েছে।
প্রবাসী ভারতীয় বালা অন্বতি মাত্র ১১ বছর বয়সে অসাধারণ বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাবিদদের স্তম্ভিত করে দিয়েছে। ও ইতিমধ্যে একটি বইও লিখেছে—এইড্স নিয়ে। বালা এ বছর কলেজে পড়ছে, বয়স মাত্র ১৩।
১৬ বছরের কিরণ কেডলায়া ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত ম্যাথামেটিক্যাল তালিম্পিয়াডে প্রথম স্থান দখলে রেখে অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে। অঙ্কের বিরল প্রতিভা কিরণের দখলে আজ বহু পুরস্কার।
আমরা আপাতভাবে যে-সব ঘটনা দেখে অলৌকিক ক্ষমতার প্রকাশ বলে মনে করি, সাধারণভাবে সে-সবই ঘটে থাকে হয় কৌশলের সাহায্যে, নতুবা আমাদের বিশেষ শরীরবৃত্তির জন্য। জাদু কৌশল ও শরীরবৃত্তি বিষয়ক বিষয়ে পিনাকীর আপাতত যতটুকু জ্ঞান আছে, তাতে কোনও অলৌকিক বাবার পথে পিনাকীর সামনে কোনও অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে দেখিয়ে পার পাওয়া অসম্ভব, পিনাকীর চ্যালেঞ্জে পরাজিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় একশো ভাগ।
এতক্ষণ যাদের কথা বললাম, তারা সকলেই এ-যুগেরই মানুষ। এ-বার যাঁর কথা বলব, তাঁর মুঠোতেই রয়েছে সবচেয়ে কম বয়সে ম্যাট্রিক অর্থাৎ দশম মান পাশ করার রেকর্ড।
১৯৩৯ সালে অর্থাৎ আজ থেকে ৫১ বছর আগে মাত্র ১০ বছর ৭ মাস বয়সে ম্যাট্রিক পাশ করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন বাণী ঘোষ। পাশ করেছিলেন প্রথম বিভাগে। বাণীদেবীর বিয়ের পর পদবি হয়েছে গুহঠাকুরতা। থাকেন কলকাতার বেহালায়। বাবা ক্যাপ্টেন জিতেন্দ্রমোহন ঘোষ ছিলেন নেপাল সরকারের চিকিৎসক। থাকতেন কাঠমাণ্ডুতে। নেপালে সে সময় মেয়েদের পড়াশোনার চল ছিল না। তাই মেয়েদের স্কুলও ছিল না। গৃহশিক্ষকের কাছেই পড়াশোনা গৃহশিক্ষক আনা হয়েছিল কলকাতা থেকে, নেপালের মহারাজা এনে দিয়েছিলেন জিতেন্দ্রমোহনের অনুরোধে। কাকা শচীন্দ্রমোহন ছিলেন কলকাতার স্মল জাজেস কোর্টের উকিল। তিনিই নিয়মিত বইপত্র ও সিলেবাস পাঠাতেন কাঠমাণ্ডুতে। পরীক্ষার তিন মাস আগে কলকাতায় এলেন। এখানেও গৃহশিক্ষকের কাছেই পড়েছিলেন। আমহার্স্ট স্ট্রিটের সিটি গার্লস স্কুল থেকে পরীক্ষা দেন।
দশ বছরে ম্যাট্রিক পাশ করেই বাণীদেবী বসে থাকেননি। ’৪১-এ মাত্র ১২ বছর বয়সে বেথুন কলেজ থেকে পাশ করেন ইণ্টারমিডিয়েট। এটাও সবচেয়ে কম বয়েসে ইণ্টারমিডিয়েট পাশের রেকর্ড। খবরটা লণ্ডন টাইমস, আনন্দবাজার, যুগান্তর-সহ বহু পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ’৪৩-এ বি এ পাশ করলেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে প্রাইভেটে পরীক্ষা দিয়ে। বয়স তখন ১৪। ভর্তি হলেন এম এ ক্লাসে। ৪৫-এ বিয়ে হল। স্বামী ইঞ্জিনিয়ার। তারপর আর পড়তে পারেননি।
বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং সাময়িকপত্রে বাণীদেবীর বহু রম্যরচনা ও গল্প প্রকাশিত হয়েছে। অংশ নিয়েছেন আকাশবাণীর কথিকায়। বাণীদেবী এখনও প্রচণ্ড কর্মক্ষম। দুই মেয়ে এক ছেলে। এক মেয়ে ডাক্তার, অন্যজন আর্কিটেক্ট একমাত্র ছেলে ইঞ্জিনিয়ার।
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশগুলোতে প্রডিজি চিহ্নিত প্রতিভার দেখা মেলে আমাদের দেশের তুলনায় বহুগুণ বেশি। প্রডিজির আবির্ভাব অনেক ঘটে, কিন্তু কালজয়ী প্রতিভার আবির্ভাবের ঘটনা একান্তই বিরল। প্রডিজি পরম বিস্ময়কর প্রতিভা বলে যাকে আমরা স্বীকৃতি দিয়ে থাকি তার প্রতিভার সঙ্গে মৌলিকত্ব যুক্ত হলে তবেই কালজয়ী প্রতিভা হিসেবে বিকশিত হওয়ার দৃঢ় সম্ভাবনা থাকে।
অনেক ক্ষেত্রে প্রতিভার দ্রুত বিকাশ-গতি শিশুকাল থেকে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এগিয়েই চলে। ফলে সমাজ পায় এক এক অসাধারণ প্রতিভা। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উত্তরকালে এদের বিকাশ-গতি মন্থর হয়ে আসে। ফলে সম্ভাবনাময় শিশু-প্রতিভা পরবর্তীকালে নেমে আসে প্রায় সাধারণের পর্যায়ে। যে হেতু শিশু বিকাশের উচ্চগতির সঙ্গে সাধারণভাবে আমরা পরিচিত নই। তাই এই ধরনের শিশু প্রতিভার সঙ্গে যখন আমরা পরিচিত হই, তখন তার অনেক কিছুই আমাদের কাছে রহস্যময়, বিস্ময়কর, ব্যাখ্যাহীন, অলৌকিক ক্ষমতার প্রকাশ, ঈশ্বরের দান, ঈশ্বরের প্রকাশ, জাতিস্মরতার প্রমাণ ইত্যাদি মনে হয়।
‘আই কিউ’ প্রসঙ্গে
মানুষ আজ অনেক এগিয়েছে, এগিয়েছে বিজ্ঞান। বহু আবিষ্কার মানবজাতিকে সমৃদ্ধ করেছে। বহু তত্ত্ব ও তথ্য অজানা অনেক কিছুকে জানতে সাহায্য করেছে। আমরা আপাত অদৃশ্য অণু-পরমাণুর অবয়ব নির্ণয় করতে পেরেছি। পেরেছি মহাকাশ গবেষণার মাধ্যমে বহু অজানাকে জানতে, অধরাকে ধরতে। অথচ আমাদের মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের বিষয়ে আমরা শতকরা দশ ভাগ খবরও জানতে পেরেছি কি না সন্দেহ। এ সন্দেহ আমার নয়, বিজ্ঞানীদের। এই মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষ থেকেই চিন্তা, বুদ্ধি, প্রজ্ঞার উৎপত্তি। উনিশ শতকে হার্বার্ট স্পেনসার, কার্ল পিয়ারসন, ফ্রান্সিস গ্যালটন প্রমুখ বিশিষ্ট বিজ্ঞানী দার্শনিকরা বুদ্ধির বিকাশ, বিবর্তন, বংশগত ভিত্তি, বুদ্ধির পরিমাপ ইত্যাদি নিয়ে বহু গবেষণা করেছেন।
ইংলণ্ডের প্রখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ চার্লস স্পিয়ারম্যান প্রথম বুদ্ধি সংক্রান্ত বিভিন্ন ধারণাকে রূপ দেন এক সুনির্দিষ্ট গাণিতিক তত্ত্বে। স্পিয়ারম্যানের ওই মতবাদ সমসাময়িক মনোবিজ্ঞানীদের কেউই প্রায় মেনে নেননি। যদিও পরবর্তীকালে তাঁর তত্ত্ব অনেকেই মেনে নিয়েছিলেন। স্পিয়ারম্যান মনে করতেন, একটি মানুষের সার্বিক বোধশক্তি জন্মগত।
এলেন ফরাসি মনোবিজ্ঞানী আলফ্রেড বিনেট। সে সময় ফ্রান্সে ছাত্রদের নিয়ে এক অভূতপূর্ব সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বিশাল সংখ্যক স্কুল ছাত্ররা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হতে থাকে। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার সম্ভাবনা কোন্ কোন ছাত্রদের বেশি, তাদের শনাক্তকরণের দায়িত্ব দেওয়া হয় বিনেটকে। উদ্দেশ্য ওই সব চিহ্নিত ছাত্রদের বিশেষ প্রশিক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষায় কৃতকার্য করা যায়। বিনেটের দায়িত্ব পাওয়ার সময় ১৯০৪-০৫ সাল। শনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে বিনেট যে অভীক্ষার প্রশ্ন তৈরি করেন, তা সবই ছিল ছাত্রদের বিভিন্ন ক্লাসের পাঠক্রমের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। স্কুলের পরীক্ষায় সাফল্য ও ব্যর্থতা বৃদ্ধি ও মেধার তারতম্যের ফল, এই ধারণা থেকেই এই অভীক্ষা প্রশ্নকে ‘বুদ্ধি অভীক্ষা’ নামে বা আই কিউ (Intelligence Quotient সংক্ষেপে I. Q) নামে অবহিত করা হতে থাকে।
‘আই কিউ’তে যে নম্বর দেওয়া হত, তার হিসেব করা হত এইভাবে প্রশ্নাবলির বিন্যাস হতো বয়স অনুপাতে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। উত্তরদাতা যে বয়সের, সেই বয়সের জন্য নির্ধারিত সঠিক উত্তর দিলে উত্তরদাতার মানসিক বয়স (mental age) ও প্রকৃত বয়স (chronological age) সমান বলে ধরে নিয়ে তাকে দেওয়া হতো ১০০ নম্বর। অর্থাৎ দশ বছরের কোনও বালক দশ বছরের জন্য নির্দিষ্ট সমস্ত প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে পারলে তাকে দেওয়া হবে ১০০। এর অর্থ দশ বছর বয়সে সাধারণ মানের ছেলেমেয়েদের যে ধরনের বুদ্ধি থাকা উচিত, তা আছে। ১০ বছরের বালকটি ২০ বছর বয়সের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নের সবগুলোর ঠিক উত্তর দিতে পারলে তার প্রাপ্য বুদ্ধি পরিমাপক সংখ্যাটি বার করতে হলে যে বয়সের উপযোগী প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে, সেই মানসিক বয়সের সংখ্যাটিকে উত্তরদাতার প্রকৃত বয়সের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে ১০০ দিয়ে গুণ করতে হবে। এই ক্ষেত্রে বালকটির বুদ্ধি পরিমাপক সংখ্যাটি হবে ২০⁄১০×১০০ = ২০০। আবার দশ বছরের বালকটি যদি কেবলমাত্র ৫ বছরের একটি শিশুর বয়সের উপযোগী প্রশ্নগুচ্ছের উত্তর দিতে সক্ষম হয়, তবে তার মানসিক বয়স ধরা হবে ৫। অতএব বালকটির বুদ্ধি পরিমাপক সংখ্যাটি হবে ৫⁄১০×১০০ = ৫০। মানসিক বয়স * প্রকৃত বয়স ×১০০ করলে বেরিয়ে আসবে বুদ্ধি পরিমাপক সংখ্যাটি।
বিশ শতকের প্রথম দশকে আলফ্রেড বিনেট যে বুদ্ধি পরিমাপক প্রশ্নাবলি তত্ত্ব হাজির করেছিলেন, বিভিন্ন সময়ে তার পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধনের নামে বিকৃতকরণের পর আমরা পেলাম বর্তমান আই কিউ-এর রূপ। ব্রিটেন ও আমেরিকার বর্ণবিদ্বেষীরা আই-কিউকে সামাজিক শ্রেণি ও জাতি গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ শুরু করল। অর্থাৎ যে আই কিউ বিনেট প্রয়োগ করা শুরু করেছিলেন ব্যক্তির ক্ষেত্রে তাই প্রযুক্ত হতে লাগলো সমষ্টির ক্ষেত্রে। বিকৃতকারীরা এই প্রয়োগের দ্বারা তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে প্রমাণ করতে চাইল, সাদা চামড়াদের আই-কিউ কালো চামড়াদের চেয়ে অনেক বেশি; আই কিউ মেধা বা বুদ্ধির পরিমাপক এবং মেধা বা বুদ্ধি অপরিবর্তনশীল। অর্থাৎ জন্মগতভাবে সাদা চামড়াদের মেধা ও বুদ্ধি কালো চামড়াদের তুলনায় অনেক উন্নত।
আই কিউ-এর প্রয়োগ সামাজিক শ্রেণি, বর্ণ বা জাতি গোষ্ঠীর উপর প্রয়োগ না করে ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেই আই কিউ অভীক্ষার প্রশ্নাবলি নির্ভরযোগ্যতা পাবে, এমনটা ভাবারও কোনও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নেই। কারণ প্রয়োজনীয় বা উপযুক্ত অনুশীলনে আই কিউ বাড়ানো সম্ভব, এমনকী, স্মৃতিকেও বাড়ানো সম্ভব। প্রতিভা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস, যা আই কিউ-এর প্রাপ্য সংখ্যা বা পরীক্ষা সাফল্যের ওপর সব সময় নির্ভর করে না। বহু ক্ষেত্রেই আই কিউ-এর সাহায্যে জিনিয়াস দূরে থাক, বুদ্ধিবৃত্তিরও কোনও হদিশ মেলে না। ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৮ সংখ্যায় ‘নিউ সায়েনটিস্ট’ পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। লেখক একজেটার Exeter বিশ্ববিদ্যালয়ের Human cognition বিভাগের অধ্যাপক এম হাও (M. Howe) সত্তর জন বিরল সংগীত প্রতিভার জীবন বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন—
জিনিয়াস তৈরি হয়, জন্মায় না
(Geniuses may be made rather than born)
আমরা পরীক্ষার সাফল্য নিয়ে বিচারে বসলে আইনস্টাইন, ডারউইন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সমরেশ বসু প্রমুখ রহু প্রতিভাধরদের ক্ষেত্রেই একেবারে বোকা বনে যেতাম।
বংশগতি বা জিন প্রসঙ্গে কিছু কথা
বিগত একশো বছরে আমরা Biological determinist (এঁরা মনে করেন মানব প্রতিভা বিকাশে জিনই সব) Cultural determinist (এঁদের মতে পরিবেশই মানব প্রতিভা বিকাশে সব) এবং Interactionist (এঁদের মতে জিন ও পরিবেশ দুইই মানব প্রতিভা বিকাশে ক্রিয়াশীল)-এদের নানা বক্তব্য ও ব্যাখ্যা শুনেছি। সে-সব নিয়ে সামান্য আলোচনায় ঢোকার প্রয়োজন অনুভব করছি।
ইদানীং মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষ নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। ব্যাপক গবেষণা চলছে মানুষের বুদ্ধির ওপর বংশগতি বা জিনের প্রভাব ও পরিবেশের সম্পর্ক নিয়ে।
আধুনিক বংশগতি বিদ্যা ও জিন বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করে আপনাদের মূল বিষয় জানার উৎসাহে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিতে চাই না। জিন আলোচনা তাই স্বল্প বাক্যে সীমাবদ্ধ রাখব।
মানুষের জন্মের শুরু ডিম্বকোষ শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত হওয়ার মুহূর্ত থেকে। নিষিক্ত কোষ দু-ভাগ হয়ে গিয়ে হয়ে যায় দু’টি কোষ। দু’টি কোষ বিভক্ত হয়ে হয় চারটি কোষে। এমনিভাবে চার থেকে আট, আট থেকে যোলো—প্রয়োজন না মেটা পর্যন্ত বিভাজন ক্রিয়া চলতেই থাকে।
বেশিরভাগ কোষের দুটি অংশ। মাঝখানে থাকে ‘নিউক্লিয়াস’ ও তার চারপাশে ঘিরে থাকে জেলির মতো জলীয় পদার্থ ‘সাইটোপ্লাজম’। নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে ‘ক্রোমোজোম’। এই ক্রোমোজোম আবার জোড়া বেঁধে অবস্থান করে। মানুষের ক্ষেত্রে প্রতিটি নিউক্লিয়াসে ২৩ জোড়া অর্থাৎ ৪৬টি ক্রোমোজোম থাকে। ক্রোমোজোম আবার এক বিশেষ ধরনের ‘ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড’-এর (Deoxyribonucleic acid) অণুর সমষ্টি-সংক্ষেপে ডি. এন. এ। দু-গাছা দড়ি পাকালে যেমন দেখতে হবে, অণুগুলো তেমনি ভাবেই পরস্পরকে পেঁচিয়ে থাকে। সব প্রাণীর বংশগতির সংকেত এই ডি এন এ-তেই ধরা থাকে। ডি এন এ থেকে আর এন এ বা (Ribonucleic acid) তৈরি হয়। আর এন এ থেকে তৈরি হয় প্রোটিন (Protein)।
২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের প্রতিটি জোড়ার ক্ষেত্রে একটি আসে পুরুষের শুক্রাণু থেকে, অন্যটি নারীর ডিম্বাণু কোষ থেকে। ক্রোমোজোমের এই জিন এককভাবে বা অন্য জিনের সঙ্গে মিলে দেহের প্রতিটি বৈশিষ্ট নির্ধারণ করে। চুলের রঙ, চোখের তারার রঙ, দেহের রঙ ও গঠন, রক্তের শ্রেণি (O, A, B, AB) ইত্যাদি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য বিশেষ বিশেষ জিনের ভূমিকা রয়েছে।
জিন বিষয়ক গবেষণার সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানীরা মনে করেন, নারী-পুরুষের মিলনের ফলে ক্রোমোজোমের সংযুক্তি ৮০ লক্ষ রকমের যে কোনও একটি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই দেখা যায়, একই পিতা-মাতার সন্তানদের মধ্যে বহু ধরনের অমিল থাকতেই পারে। লম্বা-বেঁটে, মোটা-রোগা, বাদামি চোখ, নীল চোখ, শান্ত-ছটফটে ইত্যাদি।
মা-বাবার চোখের মণি কালো, কিন্তু সন্তানের চোখের মণি কটা, মা বাবা স্বল্প দৈর্ঘ্যের মানুষ সন্তান বেজায় লম্বা, মা বাবা ফর্সা সন্তান কালো অথবা এর বিপরীত দৃষ্টান্তও প্রচুর চোখে পড়বে একটু অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেললে। বাবা সন্তানের প্রকৃত জনক হলেও এমনটা ঘটা সম্ভব। কিছু মনোবিজ্ঞানী মনে করেন, পিতা সন্তানের প্রকৃত জনক হলেও এমন ঘটা সম্ভব। একাধিক বা বহু প্রজন্ম পরে জিনের সুপ্তি ভাঙার জন্য। যেখানে বাবাই প্রকৃত সম্ভানের জনক সেখানে অনুসন্ধান চালালে প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখতে পাওয়া যাবে সন্তানটির মা অথবা বাবার পূর্বপুরুষদের কারো না কারো চোখের মণি ছিল কটা, কেউ না কেউ ছিলেন লম্বা, গায়ের রঙ ছিল কালো ইত্যাদি। আমার এক নিকট আত্মীয়ার দু-হাতের কড়ে আঙুল থেকে বেরিয়ে এসেছিল বাড়তি দুটো আঙুল। আত্মীয়ার নামটি প্রকাশ করায় অসুবিধে থাকায় আমরা এখানে বোঝার সুবিধের জন্য ধরে নিলাম, নামটি তার মাধুরী। মাধুরীর মা এবং বাবার নাম মনে করুন মিতা ও আদিত্য। মিতা ও আদিত্যের কোনও হাতেই বাড়তি আঙুল নেই। মাধুরীর এই বাড়তি আঙুলের মধ্যে আদিত্য রহস্য খুঁজে পেয়েছিলেন। মিতার চরিত্র নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। নিজেকে মাধুরীর জনক হিসেবে মেনে নিতে পারেননি। স্রেফ দুটি বাড়তি আঙুল ওদের শাস্তির পরিবারে নিয়ে এসেছিল অশান্তির আগুন।
ওঁদের অশান্তির কথা আমার কানেও এসেছিল। মিতা বাবাকে হারিয়ে ছিলেন শৈশবে। অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে জানতে পারি, মিতার বাবার দু’কড়ে আঙুল থেকেই বেরিয়েছিল বাড়তি দুটি আঙুল। একটা পুরোন ছবিও উদ্ধার করা গিয়েছিল, যাতে মিতার মা ছিলেন চেয়ারে বসে, বাবা দাঁড়িয়ে। বাঁ হাতের দৃশ্যমান কড়ে আঙুল নজর করলেই চোখে পড়ে বাড়তি আঙুল। এটুকু বললে বোধহয় খুব একটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না আদিত্যকে বুঝিয়েছিলাম, জিনের সুপ্তি ভাঙার তত্ত্বে বিশ্বাসী মনোবিজ্ঞানীদের মতামত। ওদের পরিবারে ফিরে এসেছিল শান্তি।
এই তত্ত্ব ঠিক হলে এমনটা ঘটাও অস্বাভাবিক নয়—যে পূর্বপুরুষের প্রতিভা বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, অনুকূল পরিবেশের অভাবে বিকশিত হয়নি, সেই প্রতিভাই আজ বিকশিত হয়েছে, উত্তর-পুরুষের মধ্যে।
বিস্ময়কর স্মৃতি নিয়ে দু-চার কথা
বেদ রচিত হয়েছিল ১৫০০ থেকে ১০০০ খ্রিস্টপূর্বে। সে-যুগের ঋষিরা বেদকে লিপিবদ্ধ না করে কণ্ঠস্থ করে রাখতেন। বিপুল সংখ্যক শ্লোকগুলো তাঁরা যে অসাধারণ স্মৃতির মাধ্যমে বিশুদ্ধ উচ্চারণে, সুর ও ছন্দ বজায় রেখে কণ্ঠস্থ রেখেছিলেন, তা বাস্তবিকই অতি বিস্ময়কর।
প্রাচীন যুগে স্মৃতির সাহায্যেই গুরু শিক্ষাদান করতেন। শিষ্যরাও তা স্মৃতিতেই ধরে রাখতেন এবং পরবর্তীকালে স্মৃতিকে কাজে লাগিয়েই শিক্ষা দিতেন। স্বভাবতই সে যুগের পণ্ডিত ও শিক্ষাগুরুদের স্মৃতি হয়ে উঠেছিল অসাধারণ। তাঁদেরই কিছু কিছু প্রচ্ছন্নভাবে উপস্থিত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ (recessive) জিন বিবর্তন পরম্পরায় বাহিত হয়ে বহু প্রজন্ম পরে কোনও ব্যক্তির মধ্যে এসে থাকতে পারে। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জিন ঋষিরা পেয়েছিলেন কোন পূর্বপুরুষের থেকে? আসলে এঁরা শ্লোকগুলো স্মৃতিতে ধরে রাখতে তীব্রভাবে আগ্রহী ছিলেন এবং প্রয়োজনে স্মৃতিতে ধরে রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন।
এত দীর্ঘ সময় কি জিন প্রচ্ছন্নভাবে নিজ বৈশিষ্ট্যকে বজায় রাখতে সক্ষম? এই প্রশ্নের উত্তরে এই তত্ত্বে বিশ্বাসী মনোবিজ্ঞানীরা উদাহরণ হাজির করেন—অনেক শিশু জন্মায় মনুষ্যেতর প্রাণীর অঙ্গ নিয়ে—যেমন ছোট্ট ‘লেজ’ একটি দৃষ্টান্ত। তাঁদের মতে মনুষ্যেতর যে প্রাণীটি অতীতে ছিল, তারই প্রচ্ছন্ন জিনের বর্তমান উপস্থিতিই এর জন্য দায়ী।
একান্ত প্রয়োজনে ঋষিরা বা গুরুরা শাস্ত্রকে স্মৃতিতে ধরে রাখতেন; তেমন উদাহরণ এ যুগে আমাদের দেশে বিরল হলেও অসম্ভব নয়। বিদেশে প্রচুর উদাহরণ তো আছেই। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে তুমুল আলোড়ন তুলেছে কর্নাটকের যুবক রাজেন শ্রীনিভাসন মহাদেবন। অংশ শাস্ত্রে পাই-এর অর্থ বৃত্তের পরিধিকে ব্যাস দ্বারা ভাগের ফল। এই ফল প্রায় ২২.৭ এবং মোটামুটি ধরে নেওয়া হয় সংখ্যাটা ৩.১৪। কাণ দশমিকের পর সংখ্যার শেষ নেই। ৩.১৪১৫৯২৬৩৫….এভাবে চলতেই থাকবে। রাজন ১৯৮১ সালে ৫ জুলাই গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড-এর নেওয়া পরীক্ষায় দশমিকের পর ৩১,৮১১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো একের পর এক বলে গেছে নির্ভুলভাবে স্মৃতি থেকে সময় লেগেছিল ৩ ঘণ্টা ৫৯ মিনিট। প্রতি মিনিটে রাজন বলেছিল গড়ে ১৫৬.৭টি করে সংখ্যা। কী অসম্ভব দ্রুতগতিতে বলেছিল, ভাবতে অবাক হতে হয়। এখানেই রাজনের বিস্ময়কর স্মৃতির শেষ নয়, ও উল্টো দিক থেকেও ‘পাই’ বলে যেতে পারে। রাজনের এই অনন্যসাধারণ স্মৃতি-শক্তির কার্য-কারণ জানতে আমেরিকান বিজ্ঞানীরা ১ লক্ষ ৫৭ হাজার ডলারের গবেষণা প্রকল্পে হাত দিয়েছেন।
রাজন-বিস্ময় এখানেও শেষ নয়। ‘গীতা’ রাজনের মুখস্থ। স্মৃতি থেকে বলৈ যেতে পারেন ব্র্যাডম্যানের লেখা ‘ফেয়ারওয়েল টু ক্রিকেট’ বইটির প্রতিটি লাইন, ভারতীয় রেলওয়ের ‘টাইম টেবিল’ ওঁর কণ্ঠস্থ। দূরত্ব, ভাড়া ও অন্যান্য তথা সবই স্মৃতি থেকে যখন তখন আহরণ করতে পারে।
বিদেশের প্রচুর উদাহরণ থেকে একটি দিই। জাপানের হিদেয়াকি টোমোওরি ১৯৮৭ সালে রাজনের গিনেস রেকর্ড ভেঙে বলেছে দশমিকের পর ৪০ হাজার পর্যন্ত সংখ্যা। রাজনও ছাড়ার পাত্র নয়। প্রস্তুত হচ্ছে ১ লক্ষ সংখ্যা পর্যন্ত বলে রেকর্ডকে নিরাপদে রাখতে।
পানিহাটির এক পণ্ডিতের অসাধারণ স্মৃতির কথা আজও কিংবদন্তি হয়ে রয়েছে। পণ্ডিতের নাম জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। তখন ইংরেজ আমল। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন একদিন নিত্যকার মতো গেছেন গঙ্গাস্নানে। ঘাটে তখন দুই সাহেবের মধ্যে তুমুল ঝগড়া আর হাতাহাতি চলছে। কয়েক দিনের মধ্যে দুই সাহেবের লড়াই গড়াল আদালতের কাঠগড়ায়। সাক্ষ্য দিত পণ্ডিতের ডাক পড়ে। পণ্ডিত সাক্ষ্য দিতে গিয়ে দু’জনের হুবহু ইংরেজি কথোপকথন তুলে ধরেন বিচারকের সামনে। বাদী-বিবাদী দু-জনেই পণ্ডিতের বক্তব্যের সত্যতা মেনে নিলেন। বিচারক পণ্ডিতের স্মৃতিশক্তির পরিচয় পেয়ে অবাক। বললেন, “আপনি এতদিন আগের দুজনের প্রতিটি কথা কী করে মনে রাখলেন? সত্যিই আপনার অসাধারণ স্মৃতি।”
পণ্ডিত তো সাহেবের ইংরেজি বুঝতে না পেরে এদিক-ওদিক মাথা নেড়ে পেশকারকে জিজ্ঞেস করলেন, “সাহেব কী বলছেন?”
পণ্ডিতকে পেশকার বললেন, “সে কী, আপনি ইংরেজি জানেন না?”
পণ্ডিত জানালেন, “না।”
“তাহলে দু-সাহেবের এত ঝগড়ার কথা মনে রাখলেন কী করে?”
পণ্ডিতের সরল জবাব, “সে তো শুনেছিলাম, তাই মনে ছিল।”
পেশকারের কাছে পণ্ডিতের কথা শুনে বিচারক তো আরো অবাক। এমন আশ্চর্য স্মৃতিও মানুষের হয়!
‘দুর্বল স্মৃতি’ বলে কিছু নেই, ঘাটতি শুধু স্মরণে
একটা কথা বলি। অনেকের কাছেই হয়তো অদ্ভুত শোনাবে। স্বাভাবিক মস্তিষ্ককোষের অধিকারী মানুষদের ক্ষেত্রে ‘দুর্বল স্মৃতি’ বলে কিছু নেই। আমাদের স্মৃতি-শক্তির একটা পর্যায় সংরক্ষণ (Retention)। শেষ পর্যায়ে আছে স্মরণ {Recall)। যা দেখি, যা শুনি, যেসব সংরক্ষণের বিষয়ে আমাদের কারুরই কোনও ঘাটতি নেই। স্মরণের ক্ষেত্রেই দেখা যায় আমাদের নানা ধরনের ত্রুটি।
আমার কর্মক্ষেত্রে একটি ছেলে ঘুরে ঘুরে আমাদের চা দিত। প্রতিদিন দেড়শো মানুষকে চা খাওয়াতো। কেউ নিতেন এক কাপ, কেউ দু’কাপ, কেউ অভ্যাগতকে অভ্যর্থনা জানাতে নিতেন পাঁচ কাপ। প্রতিদিনই প্রায় সকলের ক্ষেত্রেই হিসেবেরও তারতম্য হতো। কাল যিনি এক কাপ নিয়েছিলেন, আজ তিনি হয়তো নিয়েছেন তিন কাপ। ‘টি-বয়’ ছেলেটি প্রত্যেকের হিসেব স্মৃতিতে ধরে রাখত এবং প্রয়োজনের সময় স্মরণ করতে পারত। এমনকী, সে পাঁচ কাপের হিসেব দিলে যদি কেউ অভ্যাগতর কথা ভুলে তিন কাপ নিয়েছেন বলে জানাতেন, ‘টি বয়’ ছেলেটির মনে করিয়ে দিত—“এগারোটা নাগাদ নীলশার্ট সাদা প্যাণ্ট পরা এক ভদ্রলোককে এক কাপ চা খাওয়ালেন, দুটো তিরিশ নাগাদ একটা ঝাঁকড়াচুলো ইয়ং ছেলেকে খাওয়ালেন এক কাপ।” এমন অসাধারণ স্মৃতির অধিকারী ছেলেটির দৃঢ় ধারণা, ওর স্মৃতি খুবই দুর্বল তাই লেখাপড়া শেখা হয়ে ওঠেনি।
আমার শৈশব কেটেছে পুরুলিয়া জেলার ছোট্ট রেল-শহর আদ্রার বড় পলাশখোলায়। রোজকার দুধ নেওয়া হতো একটি আদিবাসী প্রবীণার কাছ থেকে। তিনি ছিলেন নিরক্ষর। কিন্তু কবে কতটা বাড়তি দুধ রাখতাম, তার পাকা হিসেব রাখতেন। ওঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, “তুমি তো আরো অনেক বাড়িতেই দুধ দাও, না লিখে সবার বাড়ির হিসেব রাখো কী করে?”
প্রবীণা জানিয়েছিলেন, “কী করে আবার? সে তো মনে থেকেই যায়!”
সে সময় প্রবীণার উত্তরে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম মা মুদির দোকান থেকে সাতটা জিনিস আনতে বললে ছ’টা আনি, একটা ভুলে যাই, আর ও এত বাড়ির এত হিসেব মনে রাখে কী করে?
এমন অনেক মা-বাবা আমার কাছে এসেছেন, যাঁদের সমস্যা সন্ধানের দুর্বল স্মৃতিশক্তি। পড়লে মনে থাকে না, পরীক্ষার ফল খারাপ হচ্ছে। সন্তানদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি এদের অনেকেই এক একটি জীবন্ত তথ্যভাণ্ডার। কেউ কপিল, রবি শাস্ত্রী, ইমরান, মুদসসর নজর, আজহারউদ্দিন, হ্যাডলি, রণতুঙ্গের ব্যাটিং, বোলিং-এর গড় বলে চলেছে। কেউ বা ব্রুস লি, সিলভেস্টার স্ট্যালোন প্রমুখের বহু তথ্য স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে অনর্গল বলে চলেছে চরম উত্তেজনার সঙ্গে। কোনও কিশোরীকে দেখেছি বোম্বের নায়ক-নায়িকাদের যত খবর জনপ্রিয় সিনেমা পত্রিকাগুলোয় প্রকাশিত হয় সবই কণ্ঠস্থ। কেউবা চিমা, চিবুজোর, সুব্রত, মনোরঞ্জনের নাড়ি-নক্ষত্রের খবর জানে। এর পরও এদের কাউকেই কি আমরা স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার জন্য অভিযুক্ত করতে পারি? ওরা সেই সব তথ্যই মনে রাখে যা মনে রাখতে ওরা খুব ভালোবাসে অথবা প্রয়োজনে বাধ্য হয়। আমাদের টি-বয়টি বা আদিবাসী দুধওয়ালি অমনি বাধ্য হয়ে মনে রাখার নজির। অমন নজির আরো বহু সহস্ৰ আছে। আমার জীবনেই অমন বহু নজির দেখেছি। আপনাদের মধ্যে অনেকে নিশ্চয়ই দেখেছেন।
মানবগুণ বিকাশে বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাব
আমাদের মানসিক জিন বৈশিষ্ট্য কিন্তু পুরোপুরি জিন বা বংশগতি প্রভাবিত নয়। পরিবেশও আমাদের মানসিক বৃত্তির ওপর বিপুলভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে।
আমরা যে দু’পায়ে
ভর দিয়ে দাঁড়াই, হাঁটি পানীয়
পশুর মতো জিব দিয়ে চেটে গ্রহণ না করে
পান করি, কথা বলে মনের ভাব প্রকাশ
করি—এ সবের কোনোটাই
জন্মগত নয়।
এইসব অতি সাধারণ মানব-ধর্মগুলোও আমরা শিখেছি, অনুশীলন দ্বারা অর্জন করেছি। শিখিয়েছে আমাদের আশেপাশের মানুষগুলোই, অর্থাৎ আমাদের সামাজিক পরিবেশ।
মানবশিশু প্রজাতিসুলভ জিনের প্রভাবে মানবধর্ম বিকশিত হবার পরিপূর্ণসম্ভাবনা (Potentialities) নিয়ে অবশ্যই জন্মায়। কিন্তু সম্ভাবনাকে বাস্তব রূপ দেয় মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-বন্ধু, শিক্ষক, অধ্যাপক, সহপাঠী, খেলার সঙ্গী, পরিচিত ও আশেপাশের মানুষরা অর্থাৎ সামাজিক পরিবেশ। এই মানবশিশুই কোনও কারণে মানুষের পরিবর্তে পশু সমাজের পরিবেশে বেড়ে উঠতে থাকলে তার আচরণে সেই পশু সমাজের প্রভাবই প্রতিফলিত হবে। আমার সমবয়স্ক বা তার চেয়ে প্রাচীন সংবাদ পাঠকদের অনেকেরই জানা নেকড়েদের দ্বারা প্রতিপালিত হওয়া ‘রামু’ ও ‘কমলার’ ঘটনা। নেকড়েদের ডেরা থেকে বালক-বালিকা দুটিকে উদ্ধার করার পর তাদের এই নামকরণ করা হয়েছিল। ওরা দুজনেই হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটত, জিভ দিয়ে চেটে জল পান করত, রান্না করা খাবার খেত না। কথাও বলতে জানত না, পরিবর্তে, নেকড়ের মতোই আওয়াজ করত। এরা মানুষের সমাজের সঙ্গে মানিয়ে না নিতে পেরে বেশি দিন বাঁচেনি।
আমার আপনার পরিবারের কোনও শিশু সভ্যতার আলো না দেখা আন্দামানের আদিবাসী জারোয়াদের মধ্যে বেড়ে উঠলে তার আচার-আচরণে, মেধায় জারোয়াদের গড় প্রতিফলন দেখতে পাব। আবার একটি জারোয়া শিশুকে শিশুকাল থেকে আপনি-আমি আমাদের সামাজিক পরিবেশ মানুষ করলে দেখতে পাব শিশুটি বড় হয়ে আমাদের সমাজের আর দশটা ছেলে-মেয়ের গড় বিদ্যে, বুদ্ধি, মেধার পরিচয় দিচ্ছে। কিন্তু একটি মানুষের পরিবর্তে একটি বনমানুষকে বা শিম্পাঞ্জিকে শিশুকাল থেকে আমাদের সামাজিক পরিবেশে মানুষ করলেও এবং আমাদের পরিবারের শিশুর মতোই লেখাপড়া শেখাবার সর্বাত্মক চেষ্টা চালালেও তাকে আমাদের সমাজের স্বাভাবিক শিশুদের বিদ্যে, বুদ্ধি, মেধার অধিকারী করতে পারব না। কারণ ওই বনমানুষ বা শিম্পাঞ্জির ভেতর বংশগতির ধারায় বংশক্রমিক গুণ না থাকায় তা অনুকূল পরিবেশ পেলেও বিকশিত হওয়া কোনওভাবেই সম্ভব নয়। অর্থাৎ মানব গুণ বিকাশে জিন ও পরিবেশ দুয়েরই প্রভাব বিদ্যমান।
আমাদের মধ্যে বংশানুক্রমিক
মানবিক গুণের বিকাশ ঘটে অনুকূল
সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশে। জিনগত
কারণে বা বংশানুক্রমিক কারণে পশুদের মধ্যে
মানবিক গুণ বা বৈশিষ্ট্য বিকশিত হওয়ার
সম্ভাবনা না থাকায় অনুকূল পরিবেশের
সাহায্যে পশুদের মানবিক গুণের
অধিকারী করা সম্ভব নয়।
এই তত্ত্ব আজ সমস্ত মনোবিজ্ঞানীর স্বীকৃতি পেয়েছে।
মানবগুণ বিকাশে পরিবেশের প্রভাব
একটি মানুষের শিশু বয়স থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত মানবিক গুণের ক্রমবিকাশের বিষয়ে উন্নততর দেশগুলোতে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। ওইসব দেশেই মনোবিজ্ঞানী ও চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এখন স্বীকার করেই নিয়েছেন—মানুষের বংশগতি সূত্রে প্রাপ্ত অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যই পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত। সেই কারণে “মানবিক গুণের বিকাশে কার প্রভাব বেশি—বংশগতি অথবা পরিবেশ।” এই জাতীয় শিরোনামের বিতর্কে ওসব দেশের বিজ্ঞানীরা আজকাল আর অবতীর্ণ হন না, এককালে যেমনটি হতেন। তবে এখনও এদেশের বহু চিকিৎসাবিজ্ঞানী বংশগতিকে অত্যধিক বা চূড়ান্ত গুরুত্ব দিতে গিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাকেই অস্বীকার করে বসেন, নাকচ করে দেন। এমনটা করার কারণ সম্ভবত, আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি বিষয়ে খোঁজ-খবর না রাখা, একসময় বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করার পর প্রতিষ্ঠা পেতেই নিশ্চল হয়ে যাওয়া।
বিজ্ঞানীরা কিন্তু বর্তমানে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, বিগত বহু হাজার বছরের মধ্যে মানুষের শারীরবৃত্তিক কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি।
এই কম্পিউটার যুগের আধুনিক সমাজের মানবশিশুর
সঙ্গে বিশ হাজার বছর আগের ভাষাহীন,
কাঁচামাংসভোজী সমাজের মানবশিশুর
মধ্যে জিনগত বিশেষ কোনও
পার্থক্য ছিল না।
অর্থাৎ সেই আদিম যুগের মানবশিশুকে এ-যুগের অতি উন্নততর বিজ্ঞানে অগ্রবর্তী কোনও সমাজে বড় করতে পারলে ওই আদিম যুগের শিশুটি আধুনিকতম উন্নত সমাজের গড় মানুষদের মতোই বিদ্যে-বুদ্ধির তাধিকারী হতো। হয় তো গবেষণা করত মহাকাশ নিয়ে অথবা সুপার-কম্পিউটার নিয়ে, অর্থাৎ অনুকূল পরিবেশে শিশুকাল থেকে বেড়ে ওঠার সুযোগ পেলে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার দেশের নিরন্ন, হতদরিদ্র, মূর্খ মানুষগুলোও হতে পারে ইউরোপ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের উন্নত প্রযুক্তবিদ্যার মধ্যে গড়ে ওঠা মানুষগুলোর সমকক্ষ। অবশ্য ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের জন্য স্বাতন্ত্র নিশ্চয়ই থাকত, যেমনটি এখনও থাকে।
বর্ণপ্রাধান্য, জাতিপ্রাধান্য, পুরুষপ্রাধান্য বজায় রাখতে বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে একধরনের প্রচার চালানো হয়, উন্নত দেশের উন্নতির মূলে রয়েছে তাদের বর্ণের, তাদের জাতির মেধাগত, বুদ্ধিগত উৎকর্ষ ও বৈশিষ্ট্য। পুরুষরাও একইভাবে প্রচার করে নারীর চেয়ে তাদের মেধাগত, বুদ্ধিগত উৎকর্ষের। বুদ্ধি মাপের নামে বুদ্ধাঙ্ককে কাজে লাগিয়ে অনেক সাদা-চামড়াই প্রমাণ করতে চায় কালো চামড়ার তুলনায় তাদের মেধা ও বুদ্ধির উৎকর্ষ। আবারও বলি এ যুগের বিজ্ঞানীরা কিন্তু যে বংশগতির তথ্য হাজির করেছেন, তাকে স্বীকার করলে বলতেই হয়, অনুকুল সুযোগ-সুবিধে না পাওয়ার দরুনই নিপীড়িত মানুষগুলো অনুকূলতার সুযোগ পাওয়া মানুষের মতো মানবিক গুণগুলোকে বিকশিত করার সুযোগ পায়নি।
এ কথাও সত্যি সামান্য অনুশীলনেই কিন্তু বুদ্ধাঙ্ক প্রচুর বাড়ানো সম্ভব—প্রজ্ঞা বা মেধাকে আদৌ না বাড়িয়েই।
রাশিয়ার শিক্ষাসংক্রান্ত আকাদেমির (Pedagogical Academy)-র পূর্ণ সদস্য এ পেট্রোভস্কি (A. Petrovasky)-র পঠিত প্রবন্ধ থেকে জানতে পারছি—স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগেই শিশুদের অনেক বিষয়ে বিশেষ শিক্ষাদানের কার্যক্রম রাশিয়ায় গ্রহণ করা হয়েছে যাতে বিস্ময়কর শিশু প্রতিভা সৃষ্টি করা যায়। দু-সপ্তাহের শিশুকে সাঁতার শেখানো হচ্ছে, স্কুলে ঢোকার আগেই তিন মিটার স্প্রিং বোর্ড থেকে ডাইভং শিখছে। অনুকূল সুযোগ অনেককেই বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যায়। অনেকে প্রতিভাকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করে পরিণত বয়সে।
পরিবেশকে আমরা প্রাথমিক দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি। এক: প্রাকৃতিক পরিবেশ, দুই: সামাজিক পরিবেশ। মানব জীবনকে এই দুই পরিবেশই প্রভাবিত করে।
মানব জীবনে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিজেদের অনুকূলে আনতে সক্ষম হলেও পৃথিবীর প্রতিটি প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে অনুকূলে আনার চেষ্টা কষ্টকল্পনা মাত্র। প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব আমাদের বিভিন্ন শারীরিক বৈশিষ্ট্যকে দিয়েছে। আমরা যে অঞ্চলে বসবাস করি তার উচ্চতা, তাপাঙ্ক, বৃষ্টিপাত, জমির উর্বরতা ইত্যাদির উপর আমাদের বহু শারীরিক বৈশিষ্ট্য নির্ভরশীল। তাইতেই গ্রাম-বাংলার মানুষের সঙ্গে পাঞ্জাবের মানুষের, হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের মানুষদের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের মানুষদের, আফ্রিকার দক্ষিণবাসী মানুষদের সঙ্গে ইউরোপের মানুষদের, মেরু অঞ্চলের মানুষদের সঙ্গে মরু অঞ্চলের মানুষদের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য দেখতে পাই।
বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন—চুলের রঙ, দেহের রঙ, চোখের তারার রঙ, দেহ গঠন ইত্যাদির মতো অনেক কিছুর পিছনেই যদিও জিন বা বংশগতির অবদান যেমন আছে, তেমনই এও সত্যি—দীর্ঘকালীন প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব শরীরগত নানা বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে এবং সেই বৈশিষ্ট্যই আবার জিনকে প্রভাবিত করে। বিজ্ঞানীরা এও স্বীকার করেন—অতি বিস্ময়কর জটিল আধুনিক কম্পিউটারের চেয়েও ডি এন-এর ক্ষমতা ও কার্যকলাপ অনেক বেশি জটিল এবং অনেক বেশি বিস্ময়কর।
প্রাকৃতিক প্রভাব যে দেহগত বৈশিষ্ট্য, দেহ বর্ণের উপর প্রভাব ফেলে থাকে, এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনায় যাওয়ার সুযোগ আমাদের নেই। পরিবর্তে বিষয়টা বুঝতে আমরা একটি দৃষ্টান্তকে ধরে নিয়ে আলোচনা করতে পারি।
যে মনুষ্যগোষ্ঠী বংশ পরম্পরায় আফ্রিকার উষ্ণ অঞ্চলে বসবাস করে, তাদের ক্ষেত্রে দেখতে পাই ধীরে ধীরে ওই অঞ্চলের অধিবাসীদের চামড়ার নীচে ঘোর কৃষ্ণ রঞ্জক পদার্থের উপস্থিতি ঘটেছে তীব্র তাপ থেকে দেহের ভেতরের যন্ত্রপাতিকে রক্ষা করতে। শরীরের ভেতরে যন্ত্রপাতিকে বাঁচানোর প্রয়োজনেই দেহবর্ণের এই পরিবর্তন বংশ পরম্পরায় ধীরে ধীরে সূচিত হয়েছে।
প্রাকৃতিক পরিবেশ শুধু আমাদের শারীরবৃত্তির ওপর নয়, মানসিকতার ওপরও প্রভাব বিস্তার করে। যে অঞ্চলের চাষি উর্বর জমির মালিক, সহজেই সেচের জল পায়, সে অঞ্চলের চাষিরা আয়াসপ্রিয় হয়ে পড়ে। হাতে বাড়তি সময় থাকার জন্য গ্রামীণ নানা সাংস্কৃতিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হতেই পারে। এমনিভাবেই তো বঙ্গ সংস্কৃতিতে এসেছে ‘বারো মাসে তেরো পার্বণ। আবার একই সঙ্গে আয়াসপ্রিয়তা আমাদের আড্ডা প্রিয়, পরনিন্দা প্রিয়, ঈর্ষাকাতর, তোষামোদ প্রিয় ইত্যাদির মতো বদ্ দোষের পাশাপাশি বড় বেশি নিরীহ, আপোষমুখি করতেই পারে, দূরে সরিয়ে রাখতে পারে লড়াকু মানসিকতাকে, যদি না সামাজিক পরিবেশের প্রভাব তাদের এইসব দোষ থেকে মুক্ত করে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বা মরু অঞ্চলের মানুষ নিজেদের ন্যূনতম খাদ্য পানীয় সংগ্রহেই, বেঁচে থাকার সংগ্রামেই দিন-রাতের প্রায় পুরোটা সময়ই ব্যয় করতে বাধ্য হয়। ফলে তাদের পক্ষে বুদ্ধি, মেধাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিনিয়োগ করার মতো সময়টুকুও থাকে না।
আবার যে অঞ্চল পেট্রলের ওপর ভাসছে, সে অঞ্চলের মানুষদের পায়ের তলাতেই তো গলানো সোনা! আয়াসহীনভাবে কিছু মানুষ এত প্রাচুর্যের অধিকারী যে ফেলে ছড়িয়েও শেষ করতে পারে না তাদের সুবিশাল আয়ের ভগ্নাংশটুকুও। শ্রমহীন, প্রয়াসহীন মানুষগুলো স্রেফ প্রকৃতির অপার দাক্ষিণ্যে ধনকুবের বনে গিয়ে ভোগসর্বস্ব হয়ে পড়ে। ভোগ থেকে কিছু সময় বুদ্ধি মেধাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিনিয়োগ করার মতো সময়টুকুও থাকে না।
আবার যে অঞ্চল পেট্রলের ওপর ভাসছে, সে অঞ্চলের মানুষদের পায়ের তলাতেই তো গলানো সোনা! আয়াসহীনভাবে কিছু মানুষ এত প্রাচুর্যের অধিকারী যে ফেলে ছড়িয়েও শেষ করতে পারে না তাদের সুবিশাল আয়ের ভগ্নাংশটুকুও। শ্রমহীন, প্রয়াসহীন মানুষগুলো স্রেফ প্রকৃতির অপার দাক্ষিণ্যে ধনকুবের বনে গিয়ে ভোগসর্বস্ব হয়ে পড়ে। ভোগ থেকে কিছু সময় বুদ্ধি মেধাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পিছনে খরচ করতেও এদের অনীহা হিমালয়ের মতো বিশাল হওয়াটাই স্বাভাবিক। কী প্রয়োজন শ্রমে, বুদ্ধি মেধা, বাড়াবার শ্রমে? জীবিকার জন্যেই তো? প্রাচুর্য যেখানে অসীম, ফুরিয়ে দেওয়ার ফুরসত নেই, সেখানে শ্রম একান্তই নিষ্প্রয়োজন। পেট্রল-খনির মালিকদের অর্থ প্রাচুর্যের ছোঁয়া লাগে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যেও। অনেক কম শ্রমে অনেক আয়াস কেনার সুযোগ গড়াগড়ি দেয় এদের হাতের মুঠোয়। প্রায় আয়াসহীন প্রাচুর্য এদেরও ভোগ-সর্বস্ব করে। ফলে মানসিক প্রগতি এই অঞ্চলের মানুষদের কাছে অধরাই থেকে যায়।
বনে-বাদাড়ে, পাহাড়ে যাদের বাসভূমি তাদের না আছে আবাদী জমি, না আছে শিল্প-কারখানা, না আছে কাজ পাওয়ার সুযোগ। বেঁচে থাকার জন্য একাস্তভাবে প্রয়োজনীয় সামান্যতম খাদ্য পানীয় জোগাড় করতে এরা প্রতিটি দিন যে সংগ্রাম করে, সেই সংগ্রামই এদের অনেক বেশি অমননীয় করে তোলে। আবার যে সব পাহাড়ি অঞ্চল ঘিরে ভ্রমণ ব্যবসা জমে উঠেছে, সে অঞ্চলের মানুষরা ভিন্নতর মানসিকতার দ্বারা পরিচালিত হয়।
প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বেড়ে ওঠা মানুষদের যে কোনও প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা অন্যদের তুলনায় বেশি থাকে।
বন্যা, খরা, ভূমিকম্প ইত্যাদির মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় দীর্ঘস্থায়ী হলে বিপর্যয়ে বিপন্ন মানুষদের অনেকেই কষ্টকর এই চাপের মুখে মানসিক রোগের শিকার হয়ে পড়েন এবং মানসিক রোগের কারণেই রক্তচাপ বৃদ্ধি, হাঁপানি, আন্ত্রিক, ক্ষত, বুক ধড়ফড়, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি রোগও অনেকেই ভোগ করেন।
মানবিক গুণের বিকাশে জনসংখ্যার ঘনত্বের কিছু প্রভাব আছে। ঘনবসতি অঞ্চলে বেড়ে ওঠা কিশোর-কিশোরীরা না পায় খেলার মাঠ, না দেখে মুক্ত আকাশ। বিরল বসতি বা পরিকল্পনা মাফিক গড়ে ওঠা অঞ্চলে যে সব ছেলেমেয়েরা বড় হয়, তারা পার্কে ঘোরে, মাঠে খেলে, নদীতে বা পুকুরে সাঁতার দেয়, নীল আকাশ, সবুজ গাছ সবই তাদের ভিন্নভাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। এখান থেকেই দেশের ভবিষ্যৎ সাঁতারু, ভবিষ্যৎ ফুটবলার, ক্রিকেটার কি অ্যাথলিট তৈরি করে।
সামাজিক পরিবেশের দু’টি ভাগ
সামাজিক পরিবেশের প্রভাব মানুষের জীবনে প্রাকৃতিক পরিবেশের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী।
সামাজিক পরিবেশকে দু’ভাগে ভাগ করলে সুবিধে হয়। এক: আর্থ সামাজিক, দুই: সমাজ-সাংস্কৃতিক।
মানব জীবনে আর্থ-সামাজিক পরিবেশের প্রভাব
দরিদ্র ও উন্নতিশীল দেশে যেখানে জীবন ধারণের ক্ষেত্রে প্রতিটি পদক্ষেপে জড়িয়ে রয়েছে বঞ্চনা ও অনিশ্চয়তা, সেখানে মানুষের জীবনে আর্থ-সামাজিক পরিবেশের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। এ-সব দেশের সংখ্যাগুরু জনসাধারণের হাতে নেই জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম অর্থ, নেই চিকিৎসার সুযোগ, নেই শিক্ষালাভের সুযোগ, আছে অপুষ্টি, আছে রোগ, আছে পানীয় জলের অভাব, আছে লজ্জা নিবারণের বস্ত্রটুকুরও অভাব, আছে বঞ্চনা, আছে দুর্নীতি, আছে শোষণ।
শৈশবে সন্তানের সবচেয়ে কাছের মানুষ মা। মায়ের স্বাস্থ্য, মায়ের মানসিকতার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সন্তানের স্বাস্থ্য ও মানসিকতা। মায়ের অপুষ্টি, মায়ের বুকের দুধ দানের অক্ষমতা, শিশু পরিচর্যার ক্ষেত্রে অক্ষমতা; যে অক্ষমতার কারণ মাকে বেঁচোকার ভাত রুটি জোগাড়েই জেগে থাকা সময়ের পুরোটাই প্রায় ব্যয় করতে হয়। সময়ের অভাব ছাড়াও থাকে অর্থের অভাবজনিত অক্ষমতা। মায়ের দরিদ্র রুগ্ণ স্বাস্থ্য ও মানসিক অবসাদ শিশুর শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক অবস্থার ওপর বিশাল প্রভাব ফেলে।
শৈশবে ও কৈশোরে শিশুরা ভোগে অপুষ্টিতে। খাদ্যাভাবে যথেষ্ট পরিমাণ প্রোটিন ও ক্যালোরির অভাবে আমাদের দেশে কিশোর-কিশোরীরা বেশির ভাগই অপরিণত দুর্বল দেহ ও মনের অধিকারী। এরা স্নায়ু দুর্বলতায় ভোগে, বোধ-শক্তি কম। আমাদের দেশে প্রতি বছর আড়াই লক্ষ শিশু ও কিশোর-কিশোরী দৃষ্টিশক্তি হারায় স্রেফ ভিটামিন ‘এ’-র অভাবে।
‘ইউনিসেফ’-এর হিসেব মতো এই দুনিয়ায় প্রতিবছর উদরাময়ে মৃত্যু হয় চল্লিশ লক্ষ শিশুর, নিউমোনিয়ায় বাইশ লক্ষ, হামে পনেরো লক্ষ, ম্যালেরিয়ায় দশ লক্ষ, ধনুষ্টঙ্কারে আট লক্ষ। অনাহারের তীব্র অসহনীয় যন্ত্রণার শিকার পনেরো কোটি শিশু—যাদের বয়স পাঁচ বছরের নিচে। ক্ষুধা আর রোগের আক্রমণে মৃত্যু পরোয়ানা লেখা জীবন্ত কঙ্কাল এইসব শিশুদের প্রায় সকলেই ভারতীয় উপমহাদেশ, লাতিন আমেরিকা এবং আফ্রিকার সাহারা মরু সন্নিহিত অঞ্চলের অধিবাসী।
বর্তমানে আমাদের দেশে দশ কোটি শিশু কোনোদিনই স্কুলের মুখ দেখেনি ও দেখবেও না—যাদের বয়স পাঁচ থেকে পনেরোর মধ্যে। ’৯০ সালে যে দশ কোটি শিশু প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হয়েছে, তাদের মধ্যে চার কোটি শিশুই প্রাথমিক শিক্ষাটুকুও শেষ করতে পারবে না স্রেফ দরিদ্রতার কারণে।
যে বয়সের শিশুরা পড়ে, খেলে, আবদার করে, অনুন্নত বা উন্নতিশীল দেশের শিশুরা সেই বয়সেই নিজের পেট চালাতে, পরিবারকে সাহায্য করতে শ্রম বিক্রি করে। এরা কাজ করে ক্ষেতে, ইটভাটায়, চায়ের দোকানে, মুদির দোকানে, গাড়ি সারাইয়ের গ্যারেজে, বিড়ি তৈরির কারিগর রূপে, গৃহভৃত্য রূপে, বাস, লরির ক্লিনার রূপে, ফেরিওয়ালা রূপে, দোকানি রূপে, ঠোঙা তৈরির শ্রমিকরূপে, আরও বহু বহু রূপে! আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার দ্বারা প্রকাশিত ১৯৭৯-এর তথ্য অনুসারে ভারতবর্ষে শিশু-শ্রমিকের সংখ্যা ১১ কোটির কাছাকাছি।
এর বাইরেও আরো কয়েক কোটি শিশু ও কিশোর-কিশোরী আছে জীবন ধারণের জন্য পাচার করে চোলাই মদ, অন্যান্য মাদকদ্রব্য, বে-আইনি বিদেশি দ্রব্য, বে-আইনি খাদ্যশস্য। কয়েক লক্ষ কিশোরী বেঁচে থাকার তাগিদে দেহ বিক্রি করে।
এরাই যখন বড় হয়, হয়ে ওঠে সমাজবিরোধী শক্তি। চুরি, ডাকাতি, লুঠ-পার্ট, ওয়াগান ভাঙা, ছিনতাই করা, দোকান-বাজার থেকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করা, সাট্টা, জুয়া, চোলাই-হেরোইন ইত্যাদির ব্যবসা করা, নির্বাচনে বুথ দখল করা, লালসা মেটাতে ধর্ষণ করা ইত্যাদি নানা সমাজবিরোধী কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। যে কোনও উপায়ে জৈবিক প্রয়োজন মেটানোই এদের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। গ্রামের কিশোরী-যুবতীদের চেয়ে শহর ও শহরতলির বস্তিবাসী ও ঘিঞ্জি
এলাকার বস্তিবাসী কিশোরী ও যুবতীদের অবস্থা অনেক বেশি খারাপ। এখানে একটি ছোট্ট ঘরে বহু মানুষকে গাদাগাদি হয়ে ভোরের সূর্যের প্রতীক্ষা করতে হয়। অনেক সময়ই এরা নারী-পুরুষের গোপন ক্রিয়াকলাপ দেখে যৌন আবেগ দ্বারা চালিত হয়। ফুটপাতবাসী কিশোরীদের অবস্থাও একই রকম। অনেক সময় ইচ্ছে না থাকলেও এবং অনেক সময় অপরিণত যৌন আবেগে এরা যৌনজীবনে প্রবেশ করে মস্তান, আত্মীয় বা পরিচিতদের হাত ধরে। বহু ক্ষেত্রেই কর্মজীবনে ঠিকাদারদের কাছে কাজ করতে গিয়ে, পরের বাড়ি রাঁধুনি ও দাসীর কাজ করতে গিয়ে অনেকের লালসা মেটাতে বাধ্য হয়।
এ দেশের রাজনৈতিক নেতারা নির্বাচনে জিতে জনগণের চেয়ে-পেশীশক্তির ওপর উত্তরোত্তর নির্ভরতা বাড়িয়েই চলেছেন। এই নির্ভরশীলতা যত বাড়বে, সমাজে সমাজবিরোধীদের অত্যাচারও ততই বাড়বে। কারণ সমাজবিরোধীরা জানে—আমরা হত্যাই করি আর ধর্ষণই করি রাজনৈতিক দাদারা তাদের স্বার্থেই এলাকা দখলের স্বার্থে আমাদের উদ্ধার করতে বাধ্য। আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় স্রেফ বেঁচে থাকার তাগিদে অসামাজিক কাজে নামতে হয়, মেয়েদের নিজেকে ও সংসারকে বাঁচাতে ইজ্জত বেচতে হয়। হরিজন নারীকে বিয়ে করার অপরাধে বর্ণহিন্দুর চাকরি হারাতে হয়। রয়েছে অস্পৃশ্যতা। রয়েছে বেগার-শ্রম। রাজনীতিকদের আশীর্বাদধন্য না হলে ‘ঋণ মেলা’য় ঋণ মেলে না। চাকরির সুযোগ সীমিত, বেকার অসীম। ফলশ্রুতি প্রায়শই খুঁটির জোরই প্রধান যোগাতা বলে বিবেচিত হয়। তাই যে মুষ্টিমেয়রা শেষপর্যন্ত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে (তা সে ‘খুঁটি’ পাকড়াবার হলেও) জীবন ধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় একটা কোনও চাকরি জোটানোই বিবেচিত হয়। ‘অপার ভাগ্য’, ‘মানতের ফল’, ‘গুরুদেবের আশীর্বাদ’, ‘গ্রহরত্নের ভেল্কি’ ইত্যাদি বলে। দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য ‘কাজের অধিকার’-এর ফাঁকা আওয়াজের পরিবর্তে যত বেকার তত কাজ থাকলে এমনটা ভাবার কোনও সুযোগ বা কারণ ঘটত না। এটাও তো সত্যি—
মানুষগুলো শুধু খাওয়ার জন্য মুখ আর পেট
নিয়ে জন্মায় না, কাজের জন্য
দুটো হাত আর মগজ ও
নিয়ে জন্মায়।
ওদের হাত ও মগজকে কাজে লাগিয়ে দেশকে সমৃদ্ধ করার দায়িত্ব যদি শাসক শ্রেণি পালন না করে, তবে অবশ্যই আমরা ধরে নিতে পারি-শাসক শ্রেণি এমনটা করছে অক্ষমতা থেকে, নতুবা শোষণের স্বার্থে। সমাজে ‘ধনী’ আর ‘গরিব’ এই ধরনের দুটি শ্রেণির মানুষ যদি থাকে, তবে ধনীরা তো নিজেদের স্বার্থেই গরিবদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য যতটুকু নিতান্তই দেওয়া প্রয়োজন, তার বেশি দিতে চাইবে না। ছলে, বলে, কৌশলে গরিবদের ন্যায্য পাওনাটুকু থেকে বঞ্চিত করবে। শোষণ না করলে কাকে বঞ্চিত করে ধনী হবে? আবার গরিবদের বাঁচতেও হবে নিজেদেরই প্রয়োজনে। গরিবরা না বাঁচালে কাদের শ্রমে ধনী হবে? কাদের শোষণ করবে? ওরা জোঁকের মতোই এমন চতুর সারল্যে নিঃশব্দে গরিষদের শোষণ করতে চায়। তাই কতই না ব্যাপক ব্যবস্থা, কতই না অসাধারণ প্রচার। ওরা আমাদের ঢালাও অধিকার দেয় চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের, শিক্ষা গ্রহণের এবং আরও অনেক কিছুর, কিন্তু অধিকার রক্ষার কোনও ব্যবস্থা করে না। গরিব ঘরের মানুষের বিনে মাইনের স্কুলে সস্তান পড়াবার স্বাদ থাকলেও সাধ্যে কুলোয় না। ঘরের ছেলে মেয়ে পড়তে গেলে রোজগার করবে কে? শিশু শ্রমের ওপর প্রায় সমস্ত দরিদ্র পরিবারকেই কিছুটা নির্ভর করতে হয়। এটাও কঠিন সত্য যে আব্রু রক্ষা করে স্কুলে যাওয়ার মতো সাধারণ পোশাকটুকুও অনেকের জোটে না। এখন এইসব নির্যাতিত মানুষদের গরিষ্ঠ অংশই মনে করেন—এসবই গত জন্মের পাপের ফল। এখনও অদ্ভুৎ রক্তে হোলি খেলা হয়। এখনও ওরা পানীয় জলের ছিটে-ফোঁটা পেতে কুয়োর কাছে অপেক্ষা করে। উচ্চবর্ণের কেউ কৃপা করে তাদের পাত্রে সামান্য জল ঢেলে দিলেই এঁরা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করেন। নতুবা পান করেন খাল বিল ডোবার দূষিত জল।
’৮১ মার্চের একটি ঘটনা। আমাদের সমিতির চাইবাসা ও জামশেদপুরের সদস্য মারফত খবর পেলাম বিহারের সিংভূম, গুমলা ও সাহেবগঞ্জ জেলায় এক অজানা রোগে আক্রান্ত হয়ে গত এক মাসের ভিতর মারা গেছে একশোর ওপর মানুষ। এটা অবশ্য সরকারি মত। আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে বহু গবাদি পশু। ইতিমধ্যে এই অসুস্থতার খবর এসেছে সংলগ্ন ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশের অঞ্চল সমূহ থেকে। সিংভূম জেলার ওপর একটা বিস্তৃত রিপোর্ট পেলাম। রোগাক্রান্তরা সকলেই আদিবাসী, দরিদ্র, নিরক্ষর ও সংস্কারাচ্ছন্ন। রোগটা এই ধরনের- রোগীর ধুম জ্বর হচ্ছে, গাঁটে গাঁটে ব্যথা, মাথায় যন্ত্রণা, ঘাড় শক্ত হয়ে যাওয়া, গলা বুজে যাওয়া এবং তিনচার দিনের মধ্যে মৃত্যু। অজানা রোগটি সম্পর্কে স্থানীয় আদিবাসীদের ধারণা—এসবই বোঙ্গার অভিশাপের ফল। রোগের শিকার যেহেতু অতি অবহেলিত সম্প্রদায় এবং এই মৃত্যুর জন্য, রোগভোগের জন্য তাদের সরকার ও সরকারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ নেই, অভিযুক্ত করছে নিজেদের ভাগ্যকেই, তাই ওসব ব্যাপার নিয়ে আর মাথা ঘামাবার প্রয়োজন বোধ করেননি। কোনও বিধানসভার প্রতিনিধি বা সাংসদ। স্থানীয় সাংসদ বাগুণ সমগ্রই মারণ রোগের খবর পেয়ে একেবারের জন্যেও ওসব অঞ্চলে যাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেননি। যে বিষয়টির প্রতিকারের সোচ্চারে কোনও দাবি ওঠেনি, ওঠেনি প্রতিবাদের ঝড়, সেখানে হেতুহীন সময় নষ্ট না করে কংগ্রেস সাংসদ নয়াদিল্লির আসল খুঁটির আশে পাশে থাকা ও তোষামোদ করাকে অনেক বেশি প্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন। তাঁর এই মনে করার পিছনেও ছিল আমাদের আর্থ-সামাজিক পরিবেশেরই প্রভাব।
গিয়েছিলাম পিনাকীকে সঙ্গী করে সিংভূম জেলার বান্দিজারি গ্রামে। চাইবাসা থেকে মাত্র পঁয়ত্রিশ কিলোমিটারের পথ। কিন্তু বেশ দুর্গম। গ্রামটি জঙ্গলের ভেতর। জঙ্গল ভেদ করে আলো আসে না, সবসময় অন্ধকার ঘেরা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসতি এলাকা। গ্রামে শ’দুই ঘর—শ’ দুই পরিবার। প্রত্যেক পরিবারেই কেউ না কেউ মারণ ব্যাধির শিকার। খাওয়ার জল চাওয়াতে যে জল এনে দিলেন সে জলের রঙ কালচে শ্যাওলার মতো, তীব্র দুর্গন্ধ। জল খেতে পারিনি। শুনলাম এ জলই ওরা পান করেন। সংগ্রহ করেন একটা প্রাচীন কুয়ো থেকে। এক বাড়ির জলের হাঁড়িতে উকি মারতেই দেখতে পেলাম জলের পোকা ও বেঙাচি।
গাঁয়ের অধিকাংশ লোকজনই দেখলাম নেশাগ্রস্ত। হাড়িয়ার নেশা আর কুসংস্কারের নেশায় ওদের ডুবিয়ে রেখে রাজনীতিকদের যখন ভালই চলে যাচ্ছে, তখন নেশা কাটাবার চেষ্টায় নামবে, এমন আকাট বোকা তাঁরা নন। অবাক বিস্ময়ে এও জানলাম, এও শুনলাম, উপজাতি বা অনুপজাতীয় কোনও নেতাই এই মারণ রোগের প্রসঙ্গ বিধানসভায় তুলে তুচ্ছ কারণে ব্যতিব্যস্ত করতে চাননি সভার শ্রদ্ধেয় প্রতিনিধিদের। ওঁরা তোলেননি কারণ ওঁরা শাসক শ্রেণি ও শোষক শ্রেণিরই প্রতিনিধি হিসেবেই নিজেকে তৈরি করে নিয়েছিলেন, ওইসব বঞ্চিত আদিবাসীদের আদৌ আপনজন ওঁরা কেউ নন। পদবি ভাঙিয়ে উপজাতি, অনুপজাতির প্রতিনিধি সেজে বিধানসভা, লোকসভা, রাজ্যসভা ইত্যাদিতে স্থান করে নিয়েছেন মাত্র।
বান্দিজারি গ্রামের মোড়ল লুগদি মুণ্ডা সঙ্গে কথা বলেছি। ওর নিজের ছেলেটিও এই অজানা রোগে মারা গেছে দিনকয়েক আগে। লুগদির ধারণা, বোঙ্গার অভিশাপেই এই মড়ক। দূরের হাসপাতালে রোগী পাঠায়নি। কারণ, পাঠিয়ে লাভ নেই। যাদের মারবার, বোঙ্গা তাদের মারবেই। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার একটিই পথ, তা হলো বোঙ্গাকে সন্তুষ্ট করা। তুষ্ট করতে তাই বোঙ্গার পুজো দেওয়া হয়েছে, বলি দেওয়া হয়েছে ছাগল-মুরগি।
বান্দিজারির কাছেই মনোহরপুর অঞ্চল। মনোহরপুর ব্লকের বারোটি গ্রামই আক্রান্ত। মনোহরপুরের আদিবাসীদেরও ধারণা বান্দিজারির আদিবাসীদের মতোই। তারাও বোঙ্গার রোষ কমাতে পুজো দিয়েছে। বাড়ি বাড়ি মরার খবর দিতে গিয়ে তাঁরা কাঁদছিলেন। না দোষারোপ করেননি সরকারের উদাসীনতার। দোষ দেননি বোঙ্গাকে পর্যন্ত। দোষ দিয়েছেন নিজেদের ভাগ্যকে।
এরকম গ্রাম আমাদের দেশে একটি দুটি বা দশটি বিশটি নয়, আছে লক্ষ লক্ষ। এমন বঞ্চিত মানুষ কোটি কোটি। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুতের আলো আর স্যাটেলাইটের মাধ্যমে টিভি যোগাযোগের বিজ্ঞাপনের বা তথ্যচিত্রে যে ছবি দূরদর্শনে প্রচারিত হয়, তার চেয়ে বহুগুণ বেশি গ্রাম দূরদর্শনে হাজির হয় না, আপনার আমার কাছে অধরাই থেকে যায়।
দূরদর্শনের পর্দায় বা বাণিজ্যিক সিনেমায় আমরা যে সুন্দর শান্ত গ্রামের ছবি দেখি, তা নিয়ে কিন্তু আমাদের দেশ নয়। আমাদের দেশ লক্ষ বান্দিজারি গ্রাম নিয়েই।
এত সবই আর্থ-সামাজিক পরিবেশেরই ফল।
এই পরিবেশের চাবিকাঠি যাদের হাতে তারা চায় না
ওইসব বঞ্চিত মানুষগুলোর নেশা কাটুক, ঘুম
ভাঙুক, নিজেদের অধিকার বিষয়ে সচেতন
হোক। এই সচেতনতা আনতে পারে
অনুকূল, সুস্থ সমাজ―
সাংস্কৃতিক পরিবেশ।
আর এও চরমতম সত্য—অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকলে চিকিৎসা লাভের স্বাধীনতা, শিক্ষা গ্রহণের স্বাধীনতা, জীবিকার স্বাধীনতা ইত্যাদি সব স্বাধীনতাই অর্থহীন রসিকতা মনে হয়।
মানব জীবনে সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রভাব
সংস্কৃতি দেশে দেশে ভিন্নতর। আবার একই দেশের ধর্মভিত্তিক, ভাষাভিত্তিক, অর্থভিত্তিক, শ্রেণিভিত্তিক অঞ্চলভিত্তিক আল আলাদা সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। আমাদের দেশের কথা ভাবুন, দেখতে পাবেন বিভিন্ন অঞ্চলের বা প্রদেশের সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে বিভিন্নতা, বৈচিত্রের অভাব নেই। দার্জিলিং জেলার সংস্কৃতির সঙ্গে মালদা জেলার সংস্কৃতির রয়েছে বহু বিভিন্নতা, যদিও দুটিই উত্তরবঙ্গেরই জেলা। মেদিনীপুর ও পুরুলিয়ার সংস্কৃতিতেও রয়েছে অনেক অসাদৃশ্য, যদিও দুটি জেলার অবস্থান পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে। আমাদের দেশের হিন্দু-মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য যেমন আছে, তেমনই আছে তামিল, গুজরাতি, ওড়িয়া, বাংলা, বিহারি ইত্যাদি ভাষাভাষীদের সংস্কৃতির মধ্যে অসাদৃশ্য। ব্রাহ্মণ সংস্কৃতির সঙ্গে শূদ্রের সংস্কৃতির যেমন অসাদৃশ্য আছে, তেমনই অসাদৃশ্য আছে ধনী, মধ্যবিত্ত ও গরিবদের গড়ে ওঠা সংস্কৃতির মধ্যেও।
আবার এই এই পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ ভারত এমনকী, অন্য রাষ্ট্র বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক উপকরণে ও গড়নে বহু সাদৃশ্য রয়েছে। তাই এ-কথাও মনে হয় ভারত-সংস্কৃতি ও বাংলাদেশ-সংস্কৃতির প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বঙ্গ-সংস্কৃতিগত মিল আমরা অনেক পাব। পাওয়াই স্বাভাবিক, কারণ আমরা মানব সংস্কৃতিরই অংশ।
আমাদের বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে নিজস্ব স্বতন্ত্র ভাষা, সঙ্গীত, শিল্প সাহিত্য, নৃত্য, নীতিবোধ, সমাজ ও পরিবার চালানোর রীতিনীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি। সুতরাং একজন মানুষ কোন দেশের কোন গোষ্ঠীর, কোন ধর্মের, কোন ভাষার, কোন শ্রেণির প্রতিনিধি, তার উপরই নির্ভর করবে মানুষটি কোন ভাষায় কথা বলবে, কী জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করবে, কোন্ শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত-নৃত্য ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত হবে, অংশ নেবে, কোন জাতীয় পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করবে; কোন রীতিনীতির দ্বারা পরিচালিত হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।
শিশুকাল থেকে আমরণ আমাদের প্রভাবিত করে আমাদের সমাঙ্গ, আমাদের সংস্কৃতি, ফলে আমরা সাধারণভাবেই সেই সমাজ ও সংস্কৃতির অংশীদার হয়ে পড়ি। শিশুকালে ও কৈশোরে আমাদের খাওয়া-দাওয়ার অভ্যাস, শিক্ষা চেতনার স্ফুরণ শুরু হয় মা-বাবা, আত্মীয়, গৃহশিক্ষক, স্কুলের শিক্ষক, পাড়া-প্রতিবেশীদের মাধ্যমে। প্রভাব পড়তে থাকে স্কুলের বন্ধু, খেলার সঙ্গী ও সমবয়সি বন্ধুদের আচরণ, ব্যবহার, কথাবার্তা, ভালোলাগা, খারাপ লাগার। গড়ে উঠতে থাকে রাজনৈতিক মতবাদ বা রাজনৈতিক দলের প্রতি সমর্থন করার মানসিকতা। কেউ জেনে বুঝে, কেউ না জেনে তার স্কুলের শিক্ষকের প্রভাবে, পরিবারের গুরুজনদের প্রভাবে অথবা কলেজের নিকটতম বন্ধুদের অথবা কোনও রাজনৈতিক সচেতন কারো প্রভাবে কোনও রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করতে শুরু করে, অথবা কেউ ব্যক্তিস্বার্থে জড়িয়ে পড়ে কলেজ-রাজনীতিতে। এমন দেখাই যায় বাবা-মায়ের রাজনৈতিক ও সমাজতাত্ত্বিক মতাদর্শকে অগ্রহণীয়, ভ্রান্ত মনে করে সন্তান বিপরীত কোনও মতাদর্শকে গ্রহণ করেছে।
আমাদের এবং অন্যান্য বহু সমাজেই শিশু, কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীদের কী পড়াশোনায়, কী জীবনে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। সন্তানের মা-বাবারাও ভীষণ ভাবেই চাইতে শুরু করেছে, এই তীব্র প্রতিযোগিতার যুগে আমার সন্তানকে টিকে থাকতে হলে ভাল হতে হবে, দারুণ কিছু ফল করতে হবে। সন্তান স্কুলে প্রথম দু-চারজনের মধ্যে না থাকলে মা-বাবারা শঙ্কিত হন। সন্তানের ওপর প্রচণ্ড চাপ দিতে থাকেন তাঁরা। এর ফল অনেক সময়ই প্রীতিপদ হয় না। অনেক মনোরোগ চিকিৎসকই এর জন্য সাধারণত অভিভাবকদের সরাসরি অভিযুক্ত করেন, অথবা পত্র-পত্রিকা ও বেতার মারফত মা-বাবাদের দোষারোপ করেন। কিন্তু তাঁরা সাধারণত কেউই বলেন না এই সামাজিক পরিবেশের জন্য আমাদের সমাজের চূড়ান্ত অনিশ্চয়তাই দায়ী। অর্থাৎ এ সবই আর্থ-সামাজিক অবস্থারই ফল।
মানুষ যে ছোট গোষ্ঠীর মধ্যে বেড়ে ওঠে, যে গোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্ম, সেই গোষ্ঠীর চোখ দিয়েই দেখে, কান দিয়ে শোনে। এ কথা যেমন সত্যি, তেমনই সত্যি, অন্য গোষ্ঠীর অনেক কিছুর সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাদের সঙ্গেও একাত্মতা অনুভব করে, তাদের আচার-ব্যবহার, ভালো লাগার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। যে পূর্ববঙ্গীয় বালক উদ্বাস্তু হয়ে এপার বাংলায় এসে ‘জবরদখল’ কলোনির বাসিন্দা, তার ক্লাসের প্রিয় বন্ধুটিই হয়তো কলকাতার কোনও বনেদি পরিবারের ছেলে। বইয়ের অভাব মেটাতে, একসঙ্গে পড়াশোনা, করতে, কলের গান শুনতে, রেডিও শুনতে ‘বাঙাল’ ছেলেটি অনেকটা সময়ই কাটায় বনেদি ‘ঘটি’র বাড়িতে। বনেদি বাড়ির অনেক কিছুই একটু একটু করে ভালো লাগতে থাকে। ভালো লাগে বনেদি সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার, মহিলাদের অন্দরমহলের আড়ালকে মনে হয় আভিজাত্যের লক্ষণ। ‘বাঙাল’দের প্রাণখোলা উচ্চস্বরে খুঁজে পায় রুচির অভাব। ইস্টবেঙ্গলের চেয়ে মোহনবাগানের জয় রক্তে বেশি তুফান তোলে।
একই ঘটনা ঘটে প্রবাসীদের ক্ষেত্রেও। তাঁরা প্রবাসভূমির মানুষদের সংস্কৃতির অনেক কিছুই গ্রহণ করেন পরম সমাদরে।
আমাদের সঙ্গীত, সাহিত্য, নাটক, চলচ্চিত্র, পত্র-পত্রিকা, দূরদর্শন আমাদের সমাজ সংস্কৃতিকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। নারী-পুরুষদের ‘ফ্রি-মিকসিং’ যখন সাহিত্যে-চলচ্চিত্রে বিপুলভাবে বিরাজ করে তখন সমাজে যৌন উচ্ছৃঙ্খলার সঙ্কট সংযোজিত হয়। ছাপার অক্ষর বা সেলুলয়েডের বুকে অপরাধ যখন অ্যাডভেঞ্চারের রূপ পায় তখন অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় তরুণ-তরুণীরা অপরাধ প্রবণতার মধ্যে উত্তেজনার আগুন পোহাতে চায়। পত্র-পত্রিকা ও প্রচার মাধ্যমগুলো যখন শোভরাজের মত ঘৃণা অপরাধীদের ‘সুপার হিরো’ করার তীব্র প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন, তখন বহু কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীরাই যে তাদের আদর্শ হিসেবে শোভরাজের মত সমাজবিরোধীদের জীবনচর্যাকেই গ্রহণ করতে চাইবে—এটাই স্বাভাবিক। দূরদর্শনে রামায়ণ, মহাভারত যেমন অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তেমনই অসাধারণ দক্ষতার চতুর চারল্যে মানুষকে আবার ভাববাদী অদৃষ্টবাদীর খাঁচায় পুড়তে চাইছে, ঘড়ির কাঁটাকে প্রগতির বিপরীতে ঘুরিয়ে দিতে চাইছে। ভক্তির প্লাবন এনে ধর্মোন্মাদনা সৃষ্টি করে মৌলবাদী শক্তিগুলোকেই উৎসাহিত করছে, শক্তিশালী করছে। প্রচার মাধ্যমগুলো নানা আজগুবি অলৌকিক ঘটনার গালগপ্পো ছেপে একতরফাভাবে সমাজ ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করছে। লটারি কালচার আজ সর্বক্লাবগ্রাসী হতে চলেছে। পুজোর আড়ম্বর ও পুজো কালচার যতই বাড়ছে ততই দেখতে পাচ্ছি যে স্বঘোষিত বস্তুবাদীরা জনগণকে সঙ্গে পেতে পুজো কালচারের সঙ্গী হয়েছিলেন, তাঁরাই স্বয়ং ঘোর আস্তিক হয়ে উঠেছেন—একটু চোখ কান খোলা রাখলে দৃষ্টান্ত মিলবে হাজার নয়, লাখে লাখে। সাংস্কৃতিক নানা ‘উৎসব’-এ হাজির হয়েছে নানা ঝাঁ-চকচকে আড়ম্বর ও হুল্লোড়। চার্টার্ড প্লেন, ফাইভ স্টার হোটেল, গ্ল্যামার কিং ও কুইনদের গা থেকে ঠিকরে পড়া আলো, ক্যামেরার ফ্ল্যাশ, কী নেই?—সুস্থ সংস্কৃতি ছাড়া অনেক কিছুই উপস্থিত।
এরই মাঝে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ পাল্টাতে তৎপর একদল। পাল্টে যাচ্ছেও। এরই পাশাপাশি সাধারণের সাংস্কৃতিক চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গ্রামে শহরে হাজির হয়েছেন আর একদল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংগ্রামী মানুষ। মানুষ পাল্টে যাচ্ছেও। এরই নাম ইতিহাস।
আমরা সমাজবদ্ধ জীব। সমাজের বিভিন্ন ঘটনার প্রতিফলন
তাই আমাদের জীবনে দেখতে পাই। আমরা
কীভাবে বিকশিত হব, তার অনেকটাই
তাই আমাদের সমাজ-সাংস্কৃতিক
পরিবেশের ওপরও
নির্ভর করে।
অবাক মেয়ে মৌসুমী ও বিস্ময়কর প্রতিভা বা Prodgy নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এতক্ষণ খুবই সংক্ষেপে যেটুকু আলোচনা করলাম তাতে অনেকে হয়তো ‘ধান ভানতে শিবের গান’-এর উদাহরণ খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু আমার কাছে এ সবই অতি প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে। কারণ আমি চাই, ভবিষ্যতে আবার কোনও বিস্ময়কর প্রতিভার খবর প্রচারিত হলে পাঠক-পাঠিকারা বিভ্রান্ত বোধ না করেন, নিজেরাই সঠিক অনুসন্ধানে নামতে পারেন, অথবা এমন বিস্ময়কর প্রতিভার পিছনে জাগতিক কারণগুলোর হদিশ অপরকেও দিতে পারেন।
অবাক মেয়ে মৌসুমীর রহস্য সন্ধানে
মৌসুমীকে জানতে, মৌসুমীর ওপর প্রাথমিক পরীক্ষা চালাতে আদ্রায় যাব ঠিক করে ফেললাম। ২৯ আগস্ট ৮৯ সন্ধ্যায় পাভলভ ইনস্টিটিউটে ডা. বাসুদেব মুখোপাধ্যায়কে পেয়ে গেলাম। ডা. মুখোপাধ্যায় আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। তিনি মৌসুমীর কাছে গিয়েছিলেন। ১৩ আগস্ট ’৮৯-র আনন্দবাজারে এঁকেই পাভলভ ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা ডা. ডি এন গাঙ্গুলির ছাত্র বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছিল। ডা. মুখোপাধ্যায়কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, “মৌসুমীকে পরীক্ষা করে কী মনে হলো আপনার?”
—”অসাধারণ। কথা বললে অবাক হয়ে যাবেন। যে কোনও প্রশ্ন করুন, কম্পিউটারের মতো উত্তর দিয়ে যাবে। আপনিও কি যাবেন নাকি?”
বললাম, “যাওয়ার ইচ্ছে আছে। আপনি কী ধরনের প্রশ্ন করেছিলেন?”
—“ও অনেক কিছু। যেমন অসাধারণ স্মৃতি, তেমনই মেধা। এইটুকুন তো বয়েস, এর মধ্যেই ডাচ্, জার্মান ও দস্তুরমতো শিখে ফেলেছে। স্মার্টলি ডাচ্, জার্মান বলে।”
এই পর্যন্ত বলেই সুর পাল্টালেন বাসুদেববাবু, “আমি মশাই শুধুই মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, আপনার মতো গোয়েন্দা নই। দেখুন, আপনি হয়তো মৌসুমীর মধ্যে অন্য কিছু খুঁজে পাবেন।”
কথায় শ্লেষের সুর স্পষ্ট। অবতার, অলৌকিক ক্ষমতাধর ও জ্যোতিষীদের দাবি যাচাই করতে সত্যানুসন্ধান করি বটে, কিন্তু গোয়েন্দাগিরি তো আমার নেশা বা পেশা নয়। এই ধরনের ঠেস দেওয়া কথা কি নিজের প্রতি আস্থাহীনতার ফল? মৌসুমীর মেধা বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, সেটা সঠিক নাও হতে পারে মনে করেই কি এমন কথা বললেন?
২ সেপ্টেম্বর ’৮৯ সালে ‘হাওড়া চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জার’ ধরলাম। সঙ্গী হলেন চিত্র-সাংবাদিক কল্যাণ চক্রবর্তী ও আমাদের সমিতির সদস্য মানিক মৈত্র। ট্রেনে সহযাত্রী হিসেবে পেলাম সুবীর চট্টোপাধ্যায় ও শঙ্কর মালাকারকে ওঁরাও মৌসুমীর বাড়িই যাচ্ছেন। ‘প্রমা সাংস্কৃতিক সংস্থা’র তরফ থেকে। ৭ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রসদনে মৌসুমীকে অভিনন্দন জানাবেন প্রমার তরফ থেকে প্রখ্যাত সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়, তারই প্রয়োজনে কিছু কথা সারতে। ইতিমধ্যে পত্র-পত্রিকায় এই অনুষ্ঠানের বিশাল বিশাল বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করেছে প্রমা।
আদ্রায় যখন পৌঁছলাম তখন সকাল ছ’টা। ঝড়িয়াডিহির রেল কোয়ার্টারে মৌসুমীদের বাড়ি পৌঁছলাম সাড়ে ছ’টায়। পাহারারত পুলিশ ঢোকার মুখে বাধা দিলেন। মৌসুমীর বাবা সাধনবাবুর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন সুধীরবাবু। সাধনবাবু ভিতরে নিয়ে গেলেন। এক ঘরের ছোট কোয়ার্টার। সামনে একফালি কাঠের জাফরিঘেরা বারান্দা। ভিতরে রান্নাঘর। ঘরে দিনের বেলাতেও আলো জ্বালতে হয়। সাধনবাবু আলাপ করিয়ে দিলেন স্ত্রী শিল্পা ও দুই মেয়ে মৌসুমী এবং মহুয়ার সঙ্গে।
সাধনবাবু টানা ঘণ্টা দুয়েক মৌসুমী বিষয়ে নানা কথা শোনালেন, দেখালেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পত্র-পত্রিকায় মৌসুমীকে নিয়ে প্রকাশিত লেখা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির কাছ থেকে আসা চিঠি ও টেলিগ্রাম। জানালেন ২১, ২২, ২৩ সেপ্টেম্বর মৌসুমীকে নিয়ে দিল্লিতে থাকবেন প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে। ‘অফিস স্পেশাল লিভ’ দিয়েছে। আমন্ত্রণের চিঠি দেখতে চাওয়ায় বললেন, চিঠি অফিসে আছে। শুনলাম আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বখ্যাত প্যারাসাইকোলজিস্ট আইন স্টিভেনসন সাধনবাবুকে চিঠি পাঠিয়ে জানিয়েছেন, মৌসুমীকে পরীক্ষা করতে আসছেন।
সাধনবাবুর কথায় মাঝেই জিজ্ঞেস করলাম, “কিছু কিছু পত্রিকায় লেখা হয়েছে মৌসুমীর জ্ঞান গ্র্যাজুয়েশন লেভেলের। মৌসুমী বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করছে। কথাগুলো কি সত্যি?”
সাধনবাবু জানালেন, “গ্র্যাজুয়েশন কী বলছেন, ওর জ্ঞান অনার্স লেভেলের। ও মাধ্যমিকে বসতে বাধ্য হচ্ছে, মাধ্যমিক না দিলে কলেজে ভর্তি করায় আইনগত অসুবিধে আছে বলে। তবে এটুকু জেনে রাখুন মাধ্যমিকে ও ফার্স্ট হবেই এবং রেকর্ড নাম্বার পেয়েই। ওর হাই স্ট্যাণ্ডার্ডের উত্তর কজন এগজামিনার বুঝবেন সে বিষয়েই সন্দেহ আছে। আর ওর গবেষণার যে সব খবর প্রকাশিত হয়েছে, তা সবই সত্যি। ওর রিসার্চের কাজ শেষ হলে পৃথিবী জুড়ে হইচই পড়ে যাবে। একটুও না বাড়িয়েই বলছি, প্রত্যাশা রাখছি ও নোবেল প্রাইজ পাবে এবং শিগগিরই।”
“কী বিষয় নিয়ে রিসার্চ করছ তুমি?” মৌসুমীকে প্রশ্নটা করলে উত্তর দিলেন সাধনবাবুই “তিনটি বিষয় নিয়ে রিসার্চ করছে। বিষয় তিনটি খুবই গোপনীয়। আর যে সব সাংবাদিক এসেছিলেন তাঁদের কাউকে বলিনি। আপনাকে বলেই শুধু বলছি—এয়ার পলিউশন, সোলার এনার্জি ও কোলকে সালফার মুক্ত করার বিষয় নিয়ে বর্তমানে গবেষণার ইচ্ছে আছে। অনেক দেশের নজর ওর ওপর রয়েছে। গবেষণার বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেলে বিদেশি শক্তি ওকে কিডন্যাপ করতে পারে। তাই এই গোপনীয়তা।”
“মৌসুমী, তোমার গবেষণার কাজ কেমন এগোচ্ছে।”
এবারের উত্তর মৌসুমীই দিল, “খুব ভালমতোই এগোচ্ছে, আশা করছি এর জন্যে নোবেল পাব আড়াই বছরের মধ্যে।”
ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে নানারকম গল্প-সল্প, হালকা রসিকতা, মুড়ি-তেলেভাজা, চা ইত্যাদির মাঝে মাঝে মৌসুমীকে যত বারই প্রশ্ন করেছি প্রায় ততবারই উত্তর দিয়েছেন সাধনবাবু এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিপ্রাদেবী। ইতিমধ্যে ওঁরা দুজনেই জানালেন বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের কথা, যাঁরা প্রত্যেকেই মৌসুমীর জ্ঞানের দীর্ঘ পরীক্ষা নিয়ে বিস্মিত হয়েছেন। আমাকে সাধনবাবু বললেন, “আপনি যে কোনও কেন্দ্রীয় বা রাজ্য মন্ত্রীর নাম জিজ্ঞেস করুন, দেখবেন পটাপট উত্তর দেবে, অথবা জিজ্ঞেস করুন না কোনও দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের নাম। অথবা অন্য কিছুও জিজ্ঞেস করতে পারেন।”
সাধনবাবু মৌসুমীকে জিজ্ঞেস করলেন, “রাজীব গান্ধী কবে প্রধানমন্ত্রী হন?”
মৌসুমী বলে গেল, “থার্টি ফার্স্ট অক্টোবর নাইনটিন এইটটি ফোর।”
সাধনবাবুর আবার প্রশ্ন, “কবে কলকাতায় জন্ম হয়েছিল?”
সাধনবাবুর চকচকে চোখে উৎসাহিত প্রশ্নে ও মৌসুমীর জবাবে সুবীরবাবু ও শঙ্করবাবু যথেষ্ট উৎসাহিত হচ্ছিলেন।
সুধীরবাবু আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, “সব ঠিক ঠিক উত্তর দিচ্ছে তো?”
বললাম, “হ্যাঁ”।
ইতিমধ্যে সাধনবাবু আরও অনেক প্রশ্নই করেছেন। আমাকেও এই ধরনের প্রশ্ন করে মৌসুমীর স্মরণ শক্তির পরীক্ষা নিতে আরও উৎসাহিত করলেন সাধনবাবু ও শিপ্রাদেবী।
না, জিজ্ঞেস করলাম না। কারণ মৌসুমীর বাবা-মা যেভাবে আমাকে পরীক্ষা নিতে মানসিকভাবে চালিত করবেন সেভাবে পরীক্ষা নিলে যে বাস্তবিকই পরীক্ষাটা আর পরীক্ষা থাকবে না, সে বিষয়ে সচেতন ছিলাম। পত্র-পত্রিকা পড়ে ও দূরদর্শনের কল্যাণে জেনেছিলাম সাধনবাবু বিজ্ঞানী। মৌসুমী তাকে বিজ্ঞান গবেষণায় সাহায্য করে। এও জেনেছি মৌসুমীর মা শিপ্রাদেবীও ভাল ছাত্রী ছিলেন। কিন্তু সাধনবাবু আর শিপ্রাদেবীর কথাবার্তায়, ব্যবহারে এই জানাকে সত্য বলে মেনে নিতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল। দুজনের বাক চাতুর্যকে তারিফ করেও বাস্তব সত্যকে টেনে আনতে বললাম, “ডাক্তার ডি এন গাঙ্গুলি আনন্দবাজারের প্রতিবেদককে বলেছেন, ‘মৌসুমীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তির পিছনে আছে সম্ভবত বহু প্রজন্ম পূর্বের কোনও সুপ্ত জিন, এই মেয়েটির মধ্যে যার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।’ এই পরিপ্রেক্ষিতে আপনার ও আপনার স্ত্রীর কাছে আপনাদের পূর্ব পুরুষদের বিষয়ে জানতে চাই।”
সাধনবাবু জানালেন, “আমাদের পূর্বপুরুষদের কেউ শ্রুতিধর ছিলেন বলে কোন দিনই শুনিনি।” আরও জানালেন চাষ-বাসই ছিল পূর্বপুরুষদের জীবিকা। সাধনবাবু ও তাঁর দাদাই প্রথম চাকরি করছেন। শিপ্রাদেবী জানালেন, “আমার বাবা ঠাকুরদারা ছিলেন বড় বড় অফিসার।”
“কী ধরনের বড় অফিসার?” প্রশ্ন করে জানতে পারলাম, বাবা ছিলেন গ্রামের পোস্ট অফিসের পোস্ট মাস্টার এবং ঠাকুরদা ছিলেন বাঁকুড়া জেলার একটি গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার।
সাধনবাবু ৬৯ সালে স্কুল ফাইনালে পাশ করেছেন থার্ড ডিভিশনে। ’৭৩-এ পাশ কোর্সের বি এস-সি পাশ করেন। বিষয় ছিল ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি, ম্যাথমেটিক্স। ’৭৮-এ ধানবাদের ফুয়েল রিসার্চ ইন্সটিটিউট-এ স্টেনোগ্রাফার হিসাবে যোগ দেন। ‘৮২-তে প্রমোশন পেয়ে জুনিয়ার ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হন এবং বর্তমানে জুনিয়র সায়েনটিস্ট পদে কাজ করছেন।
শিপ্রা দেবী স্কুল ফাইনাল পাশ করেছেন ’৭৪-এ থার্ড ডিভিশনে ’৭৮-এ পাশ কোর্সে বি এ পাশ করেন। স্টেনোগ্রাফি জানেন। ৮৬-তে ইনটিগ্রেটেড চাইল্ড ডেভলপমেণ্ট-এ সুপারভাইজার পদে যোগ দেন।
শিপ্রা দেবী লক্ষ্মীর ভক্ত। সাধনবাবু মা-কালীর শিপ্রা দেবীকে জিজ্ঞেস করলাম, “একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, আপনি নাকি মৌসুমীর জন্মের সময় দেখেছিলেন মা লক্ষ্মী শ্বেতবর্ণা সরস্বতীর রূপ নিয়ে আপনার কোলের কাছে এসে মিলিয়ে যান। ঘটনাটা কি সত্যি?”
শিপ্রা দেবী উত্তর দিলেন, “পুরোপুরি সত্যি।”
“আপনি কি বিশ্বাস করেন মৌসুমীই সরস্বতী?”
“মৌসুমী এই বয়সেই যেভাবে গবেষণার কাজ দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে চলেছে তাতে এমনটা বিশ্বাস করা কি অবাস্তব কিছু?”
“মৌসুমী কী কী ভাষা তুমি জানো?” জিজ্ঞেস করার মৌসুমীর বাবা ও মা জানালেন, বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি, জার্মান ও ডাচ ভাষা জানে।
আমার লেখা ‘অলৌকিক নয়, লৌকিক’ বইটি থেকে দুটি বাক্য একটি সাদা পাতায় লিখে ফেলল মানিক। পাতাটা এগিয়ে দিল মৌসুমীর কাছে অনুরোধ করলাম চারটি ভাষাতেই বাক্য দুটি অনুবাদ করে দিতে। সাধনবাবু বললেন, “ও পরীক্ষা করতে চাইছেন? আপনাদের এত ঝামেলার ও কষ্টের কোনও দরকার হবে না।” তাক থেকে একটা বই বের করে তার থেকে একটা পৃষ্ঠা মৌসুমীর সামনে মেলে ধরে বললেন, “এখান থেকে বাংলাটা পড়ে চারটে ভাষাতেই অনুবাদ করে কাকুদের শুনিয়ে দাও।” সাধনবাবুর রাখা বইটা তুলে নিয়ে বললাম, “হিন্দি, ডাচ, জার্মানের কিছুই বুঝব না। তাইতেই মৌসুমীকে দিয়ে লিখিয়ে নিচ্ছি। যাঁরা জানেন তাঁদের দেখিয়ে নেব।”
মৌসুমী বার কয়েক পড়ে বলল, “ইংরেজি করতে পারব না।” বললাম, “তাই লিখে দাও।” ‘English’-এর জায়গায় ‘No’ লিখে তলায় নিজের নাম সই করে দিল। হিন্দিতে প্রথম দুটি বাক্য অনুবাদ করল। ইতিমধ্যে মা বললেন, “কেন, তুমি ইংরেজি পারবে না, চেষ্টা করো না।” মৌসুমী বলল, “যুগের ইংরেজি কি?” মা বললেন, “তুমি তো জানো যুগের ইংরেজি era। চেষ্টা করো চেষ্টা করো।” মৌসুমী ‘In modern era’ পর্যন্ত লিখে প্রথম বাক্যটা অসমাপ্ত রাখল কয়েকটা ডট চিহ্ন দিয়ে। তারপর দ্বিতীয় বাক্যটা শেষ করল। Dutch লিখে লিখল No। German লিখেও No। তারপর স্বাক্ষর ও তারিখ।
সাধনবাবু আমাকে কিছু বলছিলেন। শুনছিলাম। সেই সুযোগে শিপ্রা দেবী মৌসুমীকে ইংরেজি অনুবাদের অসমাপ্ত অংশটুকুর ইংরেজিটা বলে দিয়ে লেখালেন আমাদের পাঁচ আগন্তুকের উপস্থিতিতেই। আমি শিপ্রাদেবীকে বললাম, “পরীক্ষাটা মৌসুমীর নিচ্ছি, আপনার নয়। অতএব, আপনার বলে দেওয়া অংশটা কাটুন।” অসন্তুষ্ট শিপ্রা দেবী লম্বা দাগ টেনে কাটলেন। অবশ্য না কেটে মৌসুমীর ইংরেজি জ্ঞানের প্রমাণ হিসেবে ধরে নিলেও মৌসুমীর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সামান্যতম তারতম্য ঘটত না। কারণ শিপ্রা দেবীর অনুবাদও ছিও সম্পূর্ণ ভুলে ভরা। কাটা অংশে মৌসুমী, সাধনবাবু ও সুবীর চট্টোপাধ্যায় স্বাক্ষর করলেন।
শিপ্রা দেবী আবার মুখ খুললেন, “মৌসুমী, তুমি ডাচ ও জার্মান যে সব শব্দগুলো শিখেছ সেগুলো বলে দাও তো।” বললাম, “তার কোনো প্রয়োজন নেই। ‘ধন্যবাদ’ কথাটা ২৫টি ভাষায় কেউ বলতে বা লিখতে শিখলে এই প্রমাণ হয় না যে সে ২৫টি ভাষা জানে।”
দুটি বাক্যের হিন্দি অনুবাদে মৌসুমী ভুল করেছিল ১৩টি। একথা পরের দিন জেনেছিলাম কলকাতা ৫৫-র রাষ্ট্রভাষা জ্ঞানচক্রের অধ্যক্ষ নিমাই মণ্ডলের কাছ থেকে। ইংরেজি অনুবাদের অবস্থা আরও খারাপ। প্রথম বাক্যটির কথা তো আগেই বলেছি। দ্বিতীয় বাক্যটির অনুবাদও ছিল আগাগোড়া অর্থহীন ও ভুলে ভরা।
সাধনবাবু এক সময় বলতে শুরু করলেন, “বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী ও পত্র-পত্রিকা মৌসুমীকে ‘প্রডিজি’ বলে ঘোষণা করেছে। মৌসুমীর আই কিউ অবশ্যই প্রডিজি মিনিমাম লেভেলের চেয়ে অনেক বেশি, ওর আই কিউ ২৮০।”
তৈরিই ছিলাম। নর্মান সুলিভান-এর লেখা ‘টেস্ট ইয়োর ইনটেলিজেন্স’ বই-এর ‘ইজি’ গ্রুপ থেকে তিনটি এবং ‘মোর ডিফিকাল্ট’ গ্রুপ থেকে দুটি আই কিউ দিলাম। যারা আই কিউ ক্ষমতার ন্যূনতম দাবিদার তারা প্রত্যেকেই এই পাঁচটির মধ্যে অন্তত তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম। মৌসুমী আমাদের প্রত্যেককে নিরাশ করে সাধনবাবুর দাবির চূড়ান্ত অসারতা প্রমাণ করল দুটির ক্ষেত্রে “পারব না” জানিয়ে এবং তিনটির ক্ষেত্রে ভুল উত্তর দিয়ে। তিনটি অংক দেওয়া হল। যার মধ্যে দুটি সিক্স সেভেন লেভেলের। প্রথম অংকটি—দুটি মৌলিক সংখ্যার যোগফল ৭৫। সম্ভাব্য সংখ্যা দুটি কত? ইংরেজিতে লেখা প্রশ্নটা মানিককেই পড়ে দিতে হল। মৌসুমী মানে বুঝতে পারছিল না। বাংলা মানে করে মৌলিক সংখ্যার ব্যাখ্যা করে দেওয়া হল—যে সংখ্যাকে শুধুমাত্র সেই সংখ্যা এবং ১ দিয়ে ভাগ করা যায় তাকেই বলে মৌলিক সংখ্যা।
এত বোঝানোর পরও মৌসুমী লিখল ৫২ ও ২৩। উত্তরটা অবশ্যই ভুল। কারণ ৫২কে ২, ৪, ১৩ ইত্যাদি দিয়ে ভাগ করা যায়।
দ্বিতীয় অংকটি ছিল রাম শ্যামের দোকানে এল। ৫০ টাকার জিনিস কিনে ১০০ টাকা দিল। শ্যামের কাছে খুচরো না থাকায় শ্যাম মধুর দোকান থেকে রামের ১০০ টাকা দিয়ে খুচরো এনে ৫০ টাকা রামকে দিল, রাম চলে গেল। মধু এসে জানাল ১০০ টাকাটা নকল। শ্যাম মধুকে ১০০ টাকার একটা নোট ফেরত দিতে বাধ্য হল। শ্যামের কত টাকা ক্ষতি হল?
মৌসুমী বার কয়েক প্রশ্নটা পড়ল। ওর বাবাও প্রশ্নটা বুঝিয়ে দিতে সাহায্য করলেন। মৌসুমী বাবার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, “২০০ টাকা হবে, না বাবা”।
সাধনবাবু বললেন, “তাই লেখো”। এই কথার মধ্য দিয়েই সাধনবাবু মৌসুমীকে ২০০ টাকা লেখার সংকেত দিলেন। আমি নিশ্চিত, সাধনবাবুর কাছে উত্তরটা অন্য কিছু মনে হলে “আর একটু ভাবো” জাতীয় কিছু বলে বুঝিয়ে দিতেন উত্তর ঠিক হচ্ছে না।
মৌসুমী উত্তর ২০০ টাকা লিখে স্বাক্ষর করল। এই উত্তরটাও মৌসুমী ও সাধনবাবুর ভুল হল। উত্তর হবে ১০০ টাকা। কারণ, শ্যাম মধুর কাছ থেকে ১০০ টাকা পেয়েছিল। ১০০ টাকাই ফিরিয়ে দিল। লাভ-ক্ষতি শূন্য। ক্ষতি শুধু রামকে, দেওয়া ৫০ টাকার জিনিস ও ৫০টি টাকা।
ব্যর্থতা ও অনিশ্চিত অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে সাধনবাবু বললেন, “ও ফিজিক্স, কেমিস্ট্রিতে অনার্স স্ট্যাণ্ডার্ডের। ওকে বুঝতে হলে ওইসব নিয়ে প্রশ্ন করুন।”
এমন একটা অবস্থার জন্যও তৈরি ছিলাম। পাঁচটা প্রশ্ন লিখে উত্তর দেওয়ার মতো জায়গা রেখে হাজির করলাম মৌসুমীর সামনে। প্রশ্নগুলো অবশ্যই উচ্চ মাধ্যমিক থেকে বি এস-সি পাশ কোর্স মানের। প্রথম প্রশ্ন “What is the formula of Chrome alum?”
মৌসুমী পরিষ্কার অক্ষরে লেখা ইংরেজিও পড়তে পারছিল না। পড়ে বাংলা মানে করে দেওয়ার পরও মৌসুমী উত্তরের সংকেতের আশায় বাবার মুখের দিকে চেয়ে রইল। বাবা বললেন, “মনে নেই পটাসিয়াম অ্যালার্মের ফর্মুলা।” বাবার সব চেষ্টাতে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়ে মৌসুমী লিখল “No”। করল স্বাক্ষর।
দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল “What is the clue of chemical reaction?” মৌসুমীকে পূর্ববৎ বাংলা মানে করে দিতে হল। মৌসুমী আবার দীর্ঘ সময় নিয়ে শেষপর্যন্ত লিখল “No”। করল স্বাক্ষর।
তৃতীয় প্রশ্ন “What is the equivalent weight of and acid?” প্রশ্ন নিয়ে মৌসুমী এবারও খাবি খেল। সাধনবাবু বললেন, “অ্যাসিড কাকে বলে মনে নেই।” মৌসুমী দম দেওয়া পুতুলের মতো বলে গেল, অ্যাসিড কাকে বলে। সাধনবাবু মেয়েকে বার বার করে ধরিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু মৌসুমী আবার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে লিখল “No”।
চতুর্থ প্রশ্ন “What is dynamic allotropy?” বাংলা মানে বলে দেওয়া সত্ত্বেও মৌসুমীর কিছুই বোধগম্য হল না। বাবা allotropy-র মানে ধরিয়ে দিতে বলেছিলেন, “কার্বন মানে হিরে।” না, মৌসুমী তাও উত্তর খুঁজে পায়নি। লিখেছিল “No”।
শেষ প্রশ্ন ছিল “What is the condition for the angle of contract to wet the surface?” এবার বাংলা করে দেওয়া সত্ত্বেও মৌসুমী কেন, সাধনবাবুও মানে ধরতে পারলেন না।
প্রতিটি প্রশ্ন উত্তরের পাতায় সাধনবাবু ও সাক্ষী হিসেবে সুবীরকুমার চ্যাটার্জির স্বাক্ষর করিয়ে নিলাম।
সাধনবাবুর নিজের বাড়ি রেল-কোয়ার্টারের কাছেই। সেখানেই মৌসুমীর গবেষণাগার। আমরা সকলেই গেলাম সেখানে। ছোট বাড়ি। তারই ঘরের দেওয়ালের র্যাকের দুটি সারিতে কয়েকটা টেস্ট টিউব, রাউণ্ড বটম ফ্লাস্ক ইত্যাদি সাজানো। এটাকে গবেষণাগার বললে গবেষণা ব্যাপারটাকেই ছেলেখেলা পর্যায়ে টেনে নামানো হয়।
সাধনবাবুকে বললাম, “আলোকপাত পড়ে জানলাম, মৌসুমীর টাইপের স্পিড ইংরেজিতে ১০ এবং বাংলায় ৪০। ওর টাইপের স্পিড নিয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় বিভিন্ন কথা লেখা হয়েছে। কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যে—আমার মতো অনেকেই বুঝে উঠতে পারছেন না। এ বিষয়ে আপনার মুখ থেকেই শুনতে চাই।”
সাধনবাবু জানালেন, “ইংরেজিতে ওর স্পিড মিনিটে ৬০, তবে বাংলায় ধরে ধরে টাইপ করে। কোনও স্পিড নেই।”
ইংরেজি টাইপের পরীক্ষা নিতে চাওয়ায় শিপ্রা দেবী একটা বই এগিয়ে দিলেন মেয়ের দিকে। আমি সেই বইটা সরিয়ে এগিয়ে দিলাম ‘সানডে’ পত্রিকার ২৩-২৯ জুলাই সংখ্যার পৃষ্ঠা ২১। মৌসুমী টাইপ করল ১ মিনিট সময়ে যতটা পারল। স্বাক্ষর করল নিজেই। সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর দিলেন সাধনবাবু ও সুধীরবাবু। সাধনবাবু এও লিখে দিলেন। এটা এক মিনিটে টাইপ করা হয়েছে।
দমদম মতিঝিল কলেজের গায়ে হিলনার কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট-এর ইনস্ট্রাক্টর নিরঞ্জন দাসের সঙ্গে দেখা করে মৌসুমীর করা টাইপের পাতাটা দিয়ে জানতে চেয়েছিলাম, এটার টাইপিং স্পিড কত? শ্রীদাস এই কাগজেই লিখে দিলেন স্পিড ২২। অবশ্য টাইপিং নির্ভুল ছিল না। ভুল ছিল তিনটি। আমরা কয়েকজন টাইপ শিক্ষার্থীর উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখেছি, তাঁরা ওই অংশটুকু ৩৫ থেকে ৪৫ সেকেণ্ডের মধ্যে করে দিতে পেরেছেন।
বিদায় লগ্নে মৌসুমীর বাবা অনুরোধ করলেন, মেয়ের ঐ অকৃতকার্যতাকে প্রকাশ না করার জন্য। সেই সঙ্গে ৭ সেপ্টেম্বরের সন্ধ্যায় রবীন্দ্রসদনে মৌসুমীকে অভিনন্দন জানাবার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানালেন। আমাদের পাঁচ আগন্তুককে রিকশায় তুলে দিতে এলেন সাধনবাবু। সাধনবাবুকে বললাম, “মৌসুমী খুব সুন্দর যথেষ্ট সম্ভাবনাময় একটি মেয়ে। ওর মুখ চেয়ে আপনাকে একটি অনুরোধ, ওকে না বুঝিয়ে মুখস্থ করাবেন না। এতে প্রচার হয়তো পাবেন কিন্তু এই না বুঝে মুখস্থ করার প্রবণতা ওর বুদ্ধি বিকাশের পক্ষে বাধা হতে পারে।”
৭ আগস্ট “The Telegraph” দৈনিক পত্রিকায় বক্স করে প্রকাশিত হল মৌসুমীকে পরীক্ষা করার ও তার অনুত্তীর্ণ হওয়ার খবর ৭ আগস্ট সন্ধ্যায় আমাদের সমিতির পক্ষে আমি এবং কয়েকজন ‘রবীন্দ্রসদন’-এ উপস্থিত ছিলাম মৌসুমীর অভিনন্দন অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করতে। মৌসুমীকে অভিনন্দন জানিয়ে ঘোষণা মতো অন্নদাশঙ্কর রায় কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। মামুলি প্রশ্ন। “ডু ইউ ওয়াণ্ট হ্যাপিনেস?” স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারিত হলেও ও মানে ধরতে পারল না। উত্তর দিল “আই ওয়াণ্ট টু বি এ সায়েনটিস্ট”। অন্নদাশঙ্কর হেসে ফেলে আবার প্রশ্নটা করলেন। মৌসুমী বিষয়টা ধরতে চাইছিল কিন্তু পারছিল না। পাশে বসা কৃষ্ণ ধর প্রশ্নটা বাংলা করে দিলেন। এর পরও অন্নদাশঙ্কর যেসব ইংরেজিতে প্রশ্ন করেছিলেন, তার বাংলা অনুবাদ করে দিতে হয় পাশে বসা কৃষ্ণ ধরকে।
সাধনবাবু কিছু বলতে উঠলেন। মেয়ের বিষয়ে অনেক কিছুই বললেন। আবারও ঘোষণা করলেন হিন্দি, ইংরাজি, ডাচ, জার্মান ভাষা জানে। সাধনবাবুই মেয়েকে কয়েকটা প্রশ্ন করলেন। ও উত্তর দিল। আমি প্রমা সংস্থার অন্যতম ব্যবস্থাপক সুধীরবাবু ও শংকরবাবুকে বললাম আমাকে কিছু প্রশ্ন করার অনুমতি দেবেন? সভার পরিচালক অমিতাভ চৌধুরী আমাকে অনুরোধ করলেন কোনও প্রশ্ন না করতে এবং সাধনবাবুর মিথ্যা ভাষণের প্রতিবাদ না করতে। যুক্তি হিসাবে শ্রীচৌধুরী দুটি কারণ দেখিয়েছিলেন। এক: মেয়েটি তার অভিনন্দন অনুষ্ঠানেই অপমানিত হলে চরম আঘাত পাবে। দুই: অনুষ্ঠানে গোলমাল হতে পারে। অগ্রজপ্রতিম অমিতাভ চৌধুরীর অনুরোধকে আদেশ হিসেবে শিরোধার্য করে নিয়েছিলাম।
৭ সেপ্টেম্বরের টেলিগ্রাফে মৌসুমীর বিষয়ে আমাদের সমিতির মতামত প্রকাশিত হওয়ার পরদিনই, অর্থাৎ ৮ সেপ্টেম্বরের টেলিগ্রাফে দেখলাম সাধনবাবু টেলিগ্রাফের সাংবাদিককে জানিয়েছেন, সে দিনের পরীক্ষায় খারাপ করার কারণ মৌসুমী সেদিন ‘ব্যাড মুড’-এ ছিল এবং কিছু প্রশ্ন ছিল সাধনবাবুরও বোধশক্তির অগম্য। মৌসুমীকে নাকি আমি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট লেভেলের প্রশ্ন করেছি আই কিউ-এর প্রশ্নগুলো নাকি ব্যাঙ্কের প্রবেশনারি অফিসার নিয়োগ পরীক্ষায় দেওয়া হয়। অনুবাদ করতে দিয়েছিলাম গ্র্যাজুয়েশন লেভেলের। তারপরই সাধনবাবু আবার পরীক্ষা করার জন্য আমার ও আমাদের সমিতির উদ্দেশে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন।
সেই সঙ্গে জানিয়েছেন এটা ভুললে চলবে না সে সাত বছরের শিশু এবং ১৯৯১-এ মাধ্যমিকে বসবে।
মৌসুমীর মুড ছিল না বলে সবই ভুল করেছে, এমনটা বিশ্বাস করা খুবই কঠিন। তবু আমরা সাধনবাবুর দেওয়া আবার পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছি।
বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, বেতার, দূরদর্শন, সংবাদ সরবরাহ সংস্থা সহ প্রচার মাধ্যমগুলো রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী, তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি এবং প্রধানমন্ত্রীকে লিখিত এক বক্তব্যে আমাদের সমিতির পক্ষে সভাপতি ডা. বিষ্ণু মুখার্জি জানান, মৌসুমীকে পরীক্ষা করতে কী কী ধরনের প্রশ্ন করা হয়েছিল, তারই এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে মৌসুমীর ব্যর্থতার খবর। আরও জানান, মৌসুমী লিখিতভাবেই জানিয়েছে ‘ডাচ’, ‘জার্মান’ জানে না, হিন্দি ও ইংরেজিতে অনুবাদের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে, ইংরেজিতে টাইপ করেছে ২২ স্পিডে, তাও টাইপে ভুল ছিল। মৌসুমীর বাবা দাবি করেছেন – অনুবাদ করতে দেওয়া হয়েছিল গ্র্যাজুয়েট লেভেলের, আই কিউ ছিল ব্যাঙ্কের প্রবেশনারি অফিসার নিয়োগ পরীক্ষা পর্যায়ের এবং প্রশ্নগুলো ছিল পোস্ট গ্র্যাজুয়েট লেভেলের। আমরা সেভেন, এইটের কয়েকজন ভাল ছাত্র-ছাত্রীকে ওইসব অঙ্ক, আই কিউ ও ইংরেজি অনুবাদ করতে গিয়ে দেখেছি, তারা প্রত্যেকে প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক উত্তরদানে সমর্থন হয়েছিল। মৌসুমীর বাবা আমাদের সমিতিকে জানিয়েছিলেন, মৌসুমীর জ্ঞান যদিও অনার্স গ্র্যাজুয়েটের মান অতিক্রম করেছে, কিন্তু শুধুমাত্র আইনসম্মতভাবে উচ্চশিক্ষা লাভের প্রয়োজনে ও ৯১-তে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসছে। মৌসুমীর বাবা যেহেতু জানিয়েছিলেন পরীক্ষা গ্রহণের দিন মৌসুমী মুডে ছিল না, আমরা মৌসুমীকে কিছু প্রস্তাব রাখছি।
১। মৌসুমী যখন ভাল ‘মুডে’ থাকবে তখন আবার ওর পরীক্ষা নিতে প্রস্তুত আছি। আমাদের সংস্থা মৌসুমীর এবং ওর মা-বাবার যাতায়াত খরচ পর্যন্ত বহন করবে।
২। সংবাদপত্র, দূরদর্শন, বেতার এবং অন্যান্য প্রচার-মাধ্যম, শিক্ষা দপ্তর ও অন্যান্য সরকারি দপ্তর মৌসুমীর বিষয়ে পরীক্ষা চালাতে চাইলে নিশ্চয়ই সহযোগিতা করব।
৩। মৌসুমীর মা-বাবা মৌসুমীর মেধার সত্যিকার মান বিষয়ে জনসাধারণকে অবহিত করুন।
তাঁরা কখনো বলছেন মৌসুমীর জ্ঞান অনার্স গ্র্যাজুয়েট মানের, কখনো বা বলছেন, এটা ভুললে চলবে না, মৌসুমী ৯১-এ মাধ্যমিক দেবে।
বহু ভাষাভাষী পত্র-পত্রিকায় আমাদের সমিতির এই বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। কিছু পত্র-পত্রিকা মৌসুমীকে আবার পরীক্ষায় হাজির করতে সম্ভাব্য সমস্ত রকম চেষ্টা করেছেন, কিন্তু মৌসুমীর বাবা-মা তাঁদের দাবির সত্যতা প্রমাণে এগিয়ে আসেননি!
সেই সময় সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘কোল্ডফিল্ড টাইমস’-এ প্রকাশিত একটি লেখায় বলেছিলাম—
সাধনবাবুকে একটা স্পষ্ট কথা বলি, আপনি নিজে চিন্তা-ভাবনা করে জানান মৌসুমীর জ্ঞান কোন্ পর্যায়ের। তারপর তা আবার ঘোষণা করুন। আপনিই এতদিন সংবাদ মাধ্যমগুলোকে বলেছেন মৌসুমী গবেষণা করছে, জ্ঞান অনার্স লেভেলের, দারুণ আই কিউ, দারুণ টাইপ স্পিড, বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি, জার্মান ও ডাচ জানে (যা ৭ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রসদনেও প্রকাশ্যে বলেছেন), আজ তা হলে বলছেন কেন এটা ভুললে চলবে না ও সাত বছরের মেয়ে ১৯৯১-তে মাধ্যমিক দেবে। আপনি কি মানুষকে বোকা বানাতে সেণ্টিমেণ্টে সুড়সুড়ি দিতে চাইছেন?
ওইটুকু একটা বাচ্চা মেয়ের পক্ষে ২২ স্পিডে টাইপ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়, কিন্তু ৬০-৯০-এ তোলার মিথ্যে চেষ্টা কেন? কোন উদ্দেশ্যে ডাচ, জার্মানের মিথ্যে গল্প ফাঁদছেন? কোন্ উদ্দেশ্যে ওর গায়ে অনার্স লেভেলের তকমা এঁটেছেন? গবেষক ইত্যাদি উদ্ভট কথা বলেছেন? বহু সংবাদ মাধ্যমকে এইসব কথা বলার পর এখনি কি আবার ‘বলিনি’ বলবেন ভাবছেন? আপনি কি বাস্তবিকই ওসব কথা বলেছেন, এমন প্রমাণ হাজির করলে কী করবেন ভেবেছেন কি? আবার একটি বিনীত অনুরোধ, মৌসুমীকে ‘দেবী’ বা ‘দেবশিশু’ বানিয়ে শেষ করে দেবেন না।
একটি স্বার্থান্বেষী মহল থেকে চক্রান্তও শুরু হয়ে যায় তারপরেই। প্রচার করতে থাকেন, ‘সাত বছরের বাচ্চার পিছনে লেগেছে’, ‘বাঙালি হয়ে বাঙালিকে বাঁশ দিচ্ছে’, ‘নাম কেনার জন্য চিপ স্টাণ্ট দিচ্ছে’ ইত্যাদি ইত্যাদি। এঁদের উদ্দেশে জানাই—ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি যুক্তিবাদী মানসিকতার প্রসার চায়। যুক্তি মিথ্যেকে আশ্রয় করে থাকতে পারে না। কোন রাজনৈতিক নেতা, কোন্ বিখ্যাত ব্যক্তি, কোন প্রচার মাধ্যম কাকে সমর্থন করেছে দেখে সত্যানুসন্ধানে নামা বা না নামাটা আমাদের সমিতি ঠিক করে না। যাঁরা সাত বছরের বাচ্চার প্রসঙ্গ তুলেছেন, সাত বছরের বাচ্চাটির ক্ষতি তাঁরাই করছেন। তিলে তিলে মিথ্যে প্রচারের পাঁকে ডুবিয়ে দিচ্ছেন একটা শিশুর সম্ভাবনাকে, একটা সত্যকে। ধ্বংস করতে চাইছেন একটা আন্দোলনকে, সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে। মিথ্যাচারীদের সহানুভূতি ও কৃপার উপর কোনও আন্দোলন কোনদিনই গড়ে ওঠেনি, গড়ে উঠবেও না। সমালোচকদের প্রতি আর একটা জিজ্ঞাসা—আপনারা কি চান এরপর থেকে যুক্তিবাদী সমিতি বয়স, লিঙ্গ, বাঙালি-অবাঙালি ইত্যাদি বিচার করে মিথ্যাচারিতা ধরতে নামবে? যাঁরা সমালোচনার গণ্ডি পার হয়ে ‘নাম কেনার জন্য মিথ্যা চিপ স্টাণ্ট’ বলে নোংরা কুৎসা ছড়াচ্ছেন, তাঁদের কাছে আমাদের চ্যালেঞ্জ—সাহস থাকলে সামনাসামনি প্রমাণ করুন আপনাদের বক্তব্যের সত্যতা।
আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদ্যাপন ও পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি’র অষ্টম রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বক্তা হিসেবে ১০ সেপ্টেম্বর ’৯০ আমন্ত্রিত ছিলাম। কয়েক হাজার শিক্ষক ও সাক্ষরতা কর্মীদের সোচ্চার জিজ্ঞাসা ছিল মৌসুমীকে ঘিরে। উত্তরে সব কিছুই জানিয়েছিলাম। অনেকেই প্রশ্ন করেছিলেন, মৌসুমী কি সত্যিই মাধ্যমিকে প্রথম হবে বলে মনে করেন?
বলেছিলাম, আগের দাবি প্রমাণের ক্ষেত্রে দেখেছি মৌসুমীর মা-বাবা যে ধরনের ভূমিকা পালন করেছেন, তাতে এমনটা ঘটা অস্বাভাবিক নয়, মৌসুমীর মাধ্যমিক পরীক্ষা গ্রহণ কেন্দ্রেও কিছু ফাঁক ও ফাঁকির ব্যবস্থা থেকেই যাবে, অর্থাৎ বাইরে থেকে মৌসুমীকে সহায়তা করার সুযোগ থেকেই যাবে।
১৭ সেপ্টেম্বর ’৯০-এ ‘আজকাল’ দৈনিক পত্রিকায় ‘রবিবাসর’-এ পাভলভ ইন্সটিটিউটের ডিরেক্টর ডা. ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি লেখা প্রকাশিত হলো। ১৩ আগস্ট আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর বক্তব্য থেকে তিনি অদ্ভুত রকম সরে এসেছেন লক্ষ্য করলাম। ১৭ সেপ্টেম্বর লিখছেন, “মৌসুমীর সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়নি। কাগজপত্রে তার কথা পড়েছি, আর শুনেছি আমার সহকর্মী ড: বাসুদেব মুখোপাধ্যায়ের কাছে, ড: মুখোপাধ্যায় আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। তিনি মৌসুমীর কাছে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে শুনেছি তিনি আর সকলের মতো কোনো প্রশ্ন না করে মৌসুমীকে শুধু অবজার্ভ করে গেছেন। তাঁর কাছে যা শুনেছি এবং কাগজপত্রে যা পড়েছি তাতে তো অবাক হওয়ার কিছু নেই। সকলেই বলেছেন, মৌসুমীর তাৎক্ষণিক স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর।… সুতরাং মৌসুমীকে নিয়ে হইচই করার কোনো কারণ নেই। মনে রাখতে হবে স্মৃতির সঙ্গে বুদ্ধির কোনো সম্পর্ক নেই। তার স্মৃতির মতো বুদ্ধি ততটা নেই শুনেছি।”
কিন্তু বাসুদেববাবুর কাছ থেকে শুনে ও কাগজপত্র পড়ে আনন্দবাজার প্রতিনিধিকে যে জানিয়েছিলেন, মৌসুমীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পিছনে সুপ্ত জিনের আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনার কথা। মৌসুমীর বুদ্ধির যে স্তর তাতে বিদেশে বিশেষত আমেরিকায় এর শিক্ষার ব্যবস্থা করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। এরপর এমন কী ঘটল, যাতে মাত্র ১ মাস ৪ দিনের মধ্যেই তাঁর মতো খ্যাতিমান মানসিক ব্যাধির চিকিৎসককে এমন অস্বাভাবিক রকমের মত পাল্টে বিপরীত কথা বলতে বাধ্য হলেন? তবে কি ‘দ্য টেলিগ্রাফ’ পত্রিকায় ৭ সেপ্টেম্বর ‘Prodigy fails test by rationalist’ শিরোনামের প্রকাশিত খবরটিই তাঁকে এই বিপরীত বক্তব্য প্রকাশে বাধ্য করেছে? ওই সংবাদের শেষ পংক্তিতে ছিল ‘Mr, Ghosh believes that Mousumi has an extra-ordinary memory and may have been tutored to answer questions by rote.’ অর্থাৎ ‘শ্রীঘোষ মনে করেন, মৌসুমীর স্মৃতি অসাধারণ এবং ওকে কিছু প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করানো হয়েছে।’ আর তাইতেই কি মৌসুমীর স্মৃতিকে ‘খুব প্রখর’ বলে মেনে নিয়েছেন? জানি না, প্রমা সাংস্কৃতিক সংস্থার কর্ণধার সুবীর চট্টোপাধ্যায় ও শংকর মালাকারের সঙ্গে ওই ৩ সেপ্টেম্বরই আমার মৌসুমীর স্মৃতি বিষয়ে যে সব কথাবার্তা হয়েছিল তা যদি কোনও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে ডাক্তার গাঙ্গুলির নজরে পড়ত, তারপরও ডা. গাঙ্গুলি মৌসুমীর স্মৃতি বিষয়ে নিজের বর্তমান মতে স্থির থাকতেন কি না? সুবীরবাবু ও শঙ্করবাবুকে বলেছিলাম, “মৌসুমীর যে স্মৃতি দেখে আপনারা বিস্মিত তেমন স্মৃতিশক্তি তৈরি করা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। আপনারা তো অনুষ্ঠান স্পনসর করেন। স্মৃতিশক্তির এক মজার পরীক্ষার সঙ্গে উৎসাহী দর্শকদের পরীক্ষা করতেই না হয় স্পনসর করলেন। ফেব্রুয়ারি নাগাদ রবীন্দ্রসদন ‘বুক’ করুন। হিন্দু, বেথুন, রামকৃষ্ণ মিশন, সেণ্ট জেভিয়ার্স, সাউথ পয়েণ্টের মতো ভাল স্কুলের ক্লাস এইট-নাইনের ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে ছটি আগ্রহী ভাল ছাত্র-ছাত্রী বেছে আমার হাতে তুলে দিন সাত দিনের মধ্যে অনুষ্ঠানের দিন দর্শকদের সামনে হাজির করুন মৌসুমীকে ও আমার হাতে তুলে দেওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের। হলের যে কোনও একটা অংশকে বেছে নিয়ে পঞ্চাশটির মতো দর্শকাসন রঙিন রিবন দিয়ে ঘিরে দিন। রিবন ঘেরা দর্শকদের এক এক করে নিজেদের নাম বলতে বলুন। নামগুলো টেপ-রেকর্ডারে ধরে রাখুন। তারপর মৌসুমী ও ওই ছ’টি ছেলে-মেয়েকে দর্শকদের নাম বলতে বলুন। দেখুন, মৌসুমী কতজনের ঠিক বলতে পারে। আশা রাখি আমার ছ’জনই প্রতিটি দর্শকের নাম বলতে পারবে।”
সুধীরবাবু ও শঙ্করবাবু যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়ে বলেছিলেন, “মৌসুমীরা দু-চার দিনের মধ্যেই তো কলকাতায় আসছে, সেই সময় এ বিষয়ে সাধনবাবুর সঙ্গে কথা বলে নেব। ওঁরা রাজি হলে নিশ্চয়ই স্পনসর করব।” জানুয়ারি ’৯১ অতিক্রান্ত। সুবীরবাবুদের মৌসুমীকে হাজির করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। প্রসঙ্গত জানাই, চলতি কথায় যাকে ‘স্মৃতিশক্তি বড়ানো’ বলে, সেই ‘স্মৃতি বৃদ্ধি’ বিষয়ে জানতে ও স্মৃতি বাড়াতে উৎসাহী পাঠক-পাঠিকাদের উৎসাহ মেটাতে ‘স্মৃতি প্রসঙ্গ’ নিয়ে ভবিষ্যতে একটি বই লেখার ইচ্ছে আছে।
মৌসুমী প্রসঙ্গে দুটি ঘটনার উল্লেখ করছি। প্রথম ঘটনা: ১৭ সেপ্টেম্বর ’৮৯ আজকাল পত্রিকায় সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় অমিতাভ চৌধুরী লিখলেন, ‘মৌসুমীকে নিয়ে লেখালেখি হচ্ছে বছর দুয়েক। মৌসুমী যে একটি অসাধারণ প্রতিভা সে বিষয়ে কোন কাগজেরই দ্বিমত নেই। কিন্তু যে মেয়ে বলে আগামী আড়াই বছরের মধ্যে অর্থাৎ সাড়ে ন’বছর বয়সে সে নোবেল প্রাইজ পাবে, তখন সন্দেহ হয় তার এই প্রতিভা ঠিক পথে পরিচালিত হচ্ছে তো? তাছাড়া সেদিন রবীন্দ্রসদনে সে প্রতিভার পরিচয় দিলেও অন্নদাশঙ্কর যেসব ইংরেজি প্রশ্ন করেছিলেন, তার বাংলা অনুবাদ করে দিতে হয় পাশে বসা কৃষ্ণ ধরকে।… ‘মৌসুমীর বিস্ময়কর প্রতিভা স্বীকার করে নিয়েও বলতে ইচ্ছে করছে, একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না? প্রথমত একটা রঙ্গমঞ্চে তাকে হাজির করে একমাত্র তার বাবাই অনবরত প্রশ্ন করে যাবেন এবং সে সবকটির নির্ভুল উত্তর দেবে—এর মধ্যে কোথাও কোনো গণ্ডগোল আছে বলে মনে হয়—।” ….‘মৌসুমীর প্রতিভা যাচাইয়ের ভার তার বাবার ওপর না ছেড়ে অন্য কোন বিশেষজ্ঞ কমিটির হাতে দেওয়া উচিত।’
দ্বিতীয় ঘটনা: আদ্রা থেকে ফেরার পর মৌসুমী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আগে সম্পাদক অশোক দাশগুপ্তের সঙ্গে মৌসুমীর প্রসঙ্গ নিয়ে ফোনে কথা হয়। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, মৌসুমী অন্য পত্রিকা প্রতিনিধিদের সামনে অত দ্রুততার সঙ্গে টাইপ করছে কী করে?
বলেছিলাম, “সাংবাদিকদের সামনে মৌসুমী টাইপ করেছিল নিশ্চয়ই ওর মা-বাবার এগিয়ে দেওয়া কোনও বইয়ের অংশ, যেসব অংশ ও দীর্ঘকাল ধরে টাইপ করে করে অতি অভ্যস্ত।” মৌসুমীর অসাধারণ সব উত্তরদান প্রসঙ্গে জানিয়েছিলাম, “সাধারণত মৌসুমীকে প্রশ্ন করার দায়িত্ব পালন করেন সাধনবাবু স্বয়ং। এমনভাবে উনি প্রশ্ন করা শুরু করেন যেন সাংবাদিকদের সাহায্য ও সহযোগিতা করতেই ওঁর প্রশ্নকর্তার ভূমিকা নেওয়া। সাধনবাবুর বাক্য-বিন্যাসে মোহিত হয়ে এরপর কেউ যদি সাধনবাবুর ধরনের প্রশ্ন করতে থাকেন, তবে দেখা যাবে মৌসুমী সঠিক উত্তর দিয়ে চমকে দিচ্ছে। সাধনবাবু দ্বারা চালিত না হয়ে প্রশ্ন করলে অর্থাৎ প্রকৃত পরীক্ষা করলে মৌসুমীর তেমন বিস্ময়কর প্রতিভার কিন্তু হদিশ মিলবে না।”
১৭ সেপ্টেম্বর ’৮৯ ‘আজকাল’, ‘রবিবাসর’-এর একটা পুরো পৃষ্ঠা ছিল মৌসুমীকে নিয়ে লেখায় ও ছবিতে সাজানো। তাতে ছিল মৌসুমীর এক দীর্ঘ ইণ্টারভিউ। ইণ্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের পরে। নিয়েছিলেন অরুন্ধতী মুখার্জি। শ্রীমতী মুখার্জির লেখা দুজনের কথোপকথনের কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি। “মৌসুমীকে প্রশ্ন এবার ভার নিলেন ওর বাবা-সাধন চক্রবর্তী। জিজ্ঞেস করলেন, আগামী, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কী কী উদ্দেশ্য। মৌসুমী প্রথমত, দ্বিতীয়ত করে পাঁচটি পয়েণ্ট টানা মুখস্থ বলে গেল। অদ্ভুত দ্রুত উচ্চরণে—একবারও না থেমে। আর আমি সুযোগ পেলাম না। ওর সাত বছরের মেয়ের পক্ষে নিতান্ত অনুপযুক্ত প্রশ্ন করে চললেন ইংরেজিতে। ইংরেজিতে উত্তরও। সবই সঠিক। গড়গড় করে উত্তর-কোন অ্যাকসেণ্টের বালাই না রেখেই। বিজ্ঞান, অঙ্ক, ইতিহাস সবের ওপর প্রশ্নবাণ ছুঁড়লেন তিনি। একটি বাণও বিদ্ধ করতে পারেনি তার মেয়েকে।”….“প্রায় আধ ঘণ্টা চলল বাবা মেয়ের ক্যুইজ টাইম। জিজ্ঞেস করলাম, “তুমি যা বলছ বাংলায় বলতে পারবে?”
পাশ থেকে ওর বাবা—হ্যাঁ পারবে।
ইংরেজিতে আবার বাবার প্রশ্ন, রাজীব গান্ধী করে প্রধানমন্ত্রী হন?
—থার্টি ফার্স্ট অক্টোবর নাইনটি এইট্টি ফোর।
প্রশ্নটা বাংলায় বলে বাংলায় উত্তর চাইলাম। এবারও স্মার্ট মেয়ে মৌসুমী দ্রুততার সঙ্গে বলল, থার্টি ফার্স্ট অক্টোবর নাইনটিন এইট্টি ফোর।
(এখানেও সাধারণ বোধ-বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত না হয়ে স্রেফ মুখস্থ উগরে গেছে।)
আবার ওর বাবা শুরু করলেন, কলকাতার জন্ম কবে হয়েছিল? এটা কলকাতার কত বছর? কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করে হয়েছিল?
এবার বাধা দিলাম আমরা—পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা জিনিসটা কী?
—উত্তর দেয়নি মৌসুমী।
—স্টেফি গ্রাফের নাম শুনেছ?
—১৯৮৮-র গোল্ডেন গার্ল।
—সে কী করে?
—(একটু চুপ থেকে) রান—রান করে।
পাশ থেকে উৎসাহে ওর বাবা বললেন—বল, বল, কত মিটার?
মৌসুমী এই বয়সে মৌসুমী যা পারে, অনেকেই পারে না। মৌসুমীর স্বাভাবিক বুদ্ধি বিকাশের স্বার্থেই তার মা বাবার উচিত ওই ধরনের মুখস্থ করাবার প্রবণতা থেকে বিরত থাকা। মৌসুমী জীবন্ত সরস্বতী বা সরস্বতীর অংশ, প্রমাণ করতে গিয়ে তাঁরা তাৎক্ষণিক লাভের আশায় শুধুমাত্র মানুষকে প্রতারিতই করছেন না, একটি শিশুকে তিলে তিলে শেষ করে দিচ্ছেন।
বক্সিংয়ের কিংবদন্তি মহম্মদ আলি শূন্যে ভাসেন আল্লা-বিশ্বাসে!
কিংবদন্তি বক্সার ক্যাসিয়াস ক্লে ওরফে মহম্মদ আলি তাঁর সোনালি দিনগুলোয় দুনিয়া কাঁপিয়ে ছিলেন স্ব-উদ্ভাসিত ‘রোপ-এ-ডোপ’ কৌশলে। আবার কাঁপালেন বড়দিনের ঠিক পরের দিনই।
মঙ্গলবার বড়দিনের রাতে আলি কলকাতায় পৌঁছোন। কলকাতায় আসার আগে আলি কালিকট ও বোম্বাই গিয়েছিলেন বিভিন্ন সমাজসেবী—ধর্মীয় সংস্থাকে উৎসাহিত করতে। গত কয়েকটা বছর আলিকে দেখা গেছে ধর্মীয় ও সমাজসেবী সংস্থাগুলোর পাশে। অধ্যাত্মবাদী চিন্তা যে তাঁকে যথেষ্ট নাড়া দিয়েছে, অধ্যাত্ম জগতেই যে তিনি ডুবে থাকতে চান, তা তাঁর জীবনচর্যা থেকে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না। আকাশ-ছোঁয়া উচ্চতা থেকে আলি নেমে এসেছিলেন মানুষ দেবতাদের কাছাকাছি। আর্দ্র ও শিশুদের সেবার মধ্যেই আল্লার সেবা করতে চেয়েছিলেন, আল্লাকে পেতে চেয়েছেন আপন করে। এমনই এক সন্ধিক্ষণে আলি এমন এক বিশ্ব-কাঁপানো ঘটনা ঘটালেন, যা তাঁকে রাতারাতি মানুষের দেবতা করে দিল। দীর্ঘদেহী আলি শুধুমাত্র বিশ্বাসের জোরে নিজেকে শূন্যে ভাসিয়ে রেখে বুঝিয়ে দিলেন—মাটির বুকে নেমে এসেও রয়ে গিয়েছেন সবার চেয়ে কিছুটা উপরে। যে কথা বারংবার শুনিয়েছেন পৃথিবীর মানুষকে, “আলি ইজ আলি। আই অ্যাম দ্য গ্রেটেস্ট।” সে কথাটাই আবার সবাইকে মনে করিয়ে দিলেন বক্সিং জগৎ থেকে অধ্যাত্মিক জগৎ ও সেবার জগৎ-এ প্রবেশ করে।
২৭ ডিসেম্বর ’৯০ বিভিন্ন ভাষাভাষী পত্র-পত্রিকাগুলোয় বিশাল গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হল আলির শূন্যে ভেসে থাকার অসাধারণ কাহিনি পাঠক-পাঠিকাদের কৌতূহল মেটাতে নমুনা হিসেবে ভারতবর্ষের সবচেয়ে প্রচারিত দৈনিক পত্রিকা আনন্দবাজার থেকে কয়েকটি লাইন তুলে দিচ্ছি। খবরটি প্রকাশিত হয়েছিল প্রথম পৃষ্ঠাতেই আলির বিশাল ছবি-সহ বিরাট করে।
বিশ্বাস, বিশ্বাসই সব, বলেন আলি
স্টাফ রিপোর্টার: ছয় ফুটের উপরে লম্বা, সেই অনুপাতে চওড়া শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মহম্মদ আলি। হাত দুটো ছড়িয়ে দিলেন দেহের সমান্তরালে। কয়েক সেকেণ্ড পরে উপস্থিত সাংবাদিক, আলোকচিত্রীদের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে হোটেলের ঘরে মেঝে থেকে ইঞ্চি দুয়েক উপরে উঠে গেলেন তিনি। প্রায় নির্ভার একটি পালকের মতো কয়েক সেকেণ্ড শূন্যে ভেসে থাকলেন বক্সিংয়ের কিংবদন্তি নায়ক। তার পরে মাটি ছুঁলো তাঁর পা। হতবাক দর্শকদের দিকে ফিরে অস্ফুটে বললেন আলি। বিশ্বাস, বিশ্বাসই সব, বিশ্বাসই আসল।”….. “আকাশ-ছোঁয়া উচ্চতা থেকে নেমে এসেছেন মাটির কাছাকাছি। তবু সাধারণ মানুষদের মধ্যে থেকেও নেই তিনি।” … “শূন্যে ভেসে থেকে তিনি সেটাই বোঝালেন সবাইকে।”
আলির শূন্যে ভাসা নিয়ে তোলপাড় শুরু হতেই রহস্যভেদের আমন্ত্রণ এলো ‘আজকাল’ পত্রিকার তরফ থেকে। আমন্ত্রণ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে পেলাম তাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা।
বিশ্বাসের জোরে, স্রেফ বিশ্বাসের জোরে আলি ভেসে ছিলেন!! মেনে নিতে মন চায় না। যতই প্রত্যক্ষদর্শী থাকুক, নিজের চোখে একবার না দেখে আমার পক্ষে মেনে নেওয়াটা… না, কিছুতেই পারলাম না। বারবারই মনে হতে লাগলো, ফাঁকিটা প্রত্যক্ষদর্শীদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি এ জাতীয় ঘটনার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনায় কিছু কিছু ফাঁক থেকেই যায়। তবু প্রাথমিক একটা ধারণা গড়ে তুলতে একাধিক প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছি। এক সাংবাদিক বললেন, “আলি একটা অন্য ব্যাপার। উনি যখন এসে দাঁড়ালেন, ওঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হল ওঁর সারা শরীর থেকে যেন একটা জ্যোতি বেরুচ্ছে। এখনও ভাবতে গেলে গা শিরশির করে। ও এখন অন্য জগতের মানুষ। খুব কাজ থেকে ওঁর শূন্যে ভাসা দেখেছি। না স্টেজ, না আলোর কারসাজি, উনি শূন্যে ভেসে রইলেন। না না, এতে কোনও কৌশল-টৌশলের ব্যাপার ছিল না।”
আর এক সাংবাদিক বন্ধু জানালেন, “আলি তো অলৌকিক ক্ষমতার দাবি করেননি। যোগ ক্ষমতার দ্বারা তো এমনটা করা যায়ই। আমাদের দেশে এ তো নতুন কিছু নয়। অনেক সাধু সন্তুরাই যোগ ক্ষমতায় এমনটা ভেসে দেখিয়েছেন। এমনটা যে ভেসে থাকা যায় সে তো প্রমাণ হয়েই গেছে।”
এক সাহিত্যিক বন্ধু তো একটা গল্পই শোনালেন। একটি বিখ্যাত সাধকদের জীবন-গ্রন্থে নাকি আছে, কোনও এক সাধু গভীর ঈশ্বর বিশ্বাসে ভর করে হেঁটে উত্তাল নদী পার হচ্ছিলেন। সাধু হেঁটে চলেছেন ঈশ্বর বিশ্বাসে বুঁদ হয়ে, নেশাগ্রস্ত মানুষের মতো। পাড়ের কাছাকাছি পৌঁছে হঠাৎ সাধু হুঁশ ফিরে পেলেন-আমি এতটা পায়ে হেঁটে চলে এসেছি। শেষ পথটুকু পার হতে পারব তো? যেমনি ভাবা, অমনি টুপ করে এক টুকরো পাথরের মতোই ডুবে গেলেন। আসলে বিশ্বাসই সব। ঈশ্বরে অন্ধ বিশ্বাস রাখলে অমন অনেক কিছুই ঘটে, ঘটানো যায়—যেগুলো সাধারণ মানুষদের চোখে ‘অলৌকিক’ বলেই প্রতিভাত হয়।
স্টেজে নয়, হোটেলের ফ্লোরে মোট দু’বার সাংবাদিকদের শূন্যে ভেসে দেখিয়েছেন আলি। কী এমন কৌশল!! যার ফলে একজন মানুষ একটু একটু করে উঠে পড়েন শূন্যে? যে সব তথাকথিত অবতাররা শূন্যে ভাসেন বলে কথিত আছে তাঁদের সে-সব কৌশল আমার অজানা নয় (উৎসাহী পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির জন্য জানাই ‘অলৌকিক নয়, লৌকিক’-এর প্রথম খণ্ডে সেইসব গোপন কৌশল নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি বহু ছবি সহ)। তাঁরা কেউই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শূন্যে উঠে পারেননি। এ এক নতুনভাবে শূন্যে ভাসা, নতুন পদ্ধতিতে শূন্যে ভাসা।
২৯ ডিসেম্বর শনিবার দুপুরে আমাদের সমিতির জ্যোতি মুখার্জিকে সঙ্গী করে তাজ বেঙ্গল হোটেলে পৌঁছলাম। তখন হোটেলের লাউঞ্জে আলির খবর সংগ্রহ করতে সাংবাদিক ও চিত্র-সাংবাদিকদের ভিড়। শুনলাম, তিনদিন ধরে সকাল থেকে রাত এঁরা ঘাঁটি গেড়ে রয়েছেন। কিন্তু আলিকে যাঁরা এদেশে এনেছেন তাঁদের হার্ডেল টপকে ৩২৪ নম্বর ঘরে ঢুকে আলির সঙ্গে আলাপ জমাবার সুযোগ পাননি কেউই। আলি একতলার রেস্তোরাঁয় এলে বা বাইরে বেরুলে আলিকে ফিল্ম বন্দি করার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে বটে, কিন্তু নিশ্ছিদ্র পাহারা এড়িয়ে কথা বলার তেমন সুযোগ জুটছে না।
‘আজকাল’-এর সাংবাদিক অনুরূপ ভৌমিক ও চিত্র-সাংবাদিক সজল মুখার্জির দেখা পেলাম হোটেল লাউঞ্জেই। তারপর প্রতীক্ষা। আলির মুখোমুখি হতে পারলেও তাঁর মতো বিশাল ব্যক্তিত্ব আমার অনুরোধকে মর্যাদা দিয়ে আবার শূন্যে ভেসে দেখাবেন কি না, এ বিষয়ে আমারও সন্দেহ ছিল। কিন্তু এখানে এসে দেখছি—প্রবেশাধিকারের হার্ডেলই এভারেস্টের উচ্চতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।
এরই ফাঁকে আলাপ হল আলির জীবনী নিয়ে গড়ে ওঠা ‘দ্য হোল স্টোরি’র পরিচালক লিণ্ডসে কেনেল-এর সঙ্গে। জানালেন, ‘দ্য হোল স্টোরি’র শুটিং উপলক্ষেই তাঁর ভারতে আগমন। ছবিটির প্রযোজক মহমেডান ক্লাবের সহ-সভাপতি মির মহম্মদ ওমরের দাদা। খরচ হবে কয়েক লক্ষ ডলার। সারা পৃথিবীতে ছবিটি মুক্তি পাবে।
মির মহম্মদ ওমরের সহযোগিতায় ৩২৪ নম্বর ঘরে আলির মুখোমুখি হলাম। তখনও দুটো হার্ডেল অতিক্রম করা বাকি। এক: আলির শূন্যে ভাসা দেখা, দুই: শূন্যে ভাসার রহস্যভেদ। শেষ পর্যন্ত কি ঘটেছিল? না, আমি আর মুখ খুলছি না। আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি ৩০ ডিসেম্বর ‘আজকাল’-এর প্রথম পৃষ্ঠায়। আলি এবং আমার ছবি সহ প্রতিবেদনটি থেকে কিছুটা অংশ তুলে দিচ্ছি।
ফেরার দিন ম্যাজিক দেখলেন, দেখালেনও
আজকালের প্রতিবেদন: মহম্মদ আলি আবার শূন্যে ভেসে উঠলেন। একবার নয়, পাঁচবার। এবং এবার পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল ব্যাপারটা অলৌকিক নয়। যতবার শূন্যে উঠলেন একটা দিকে কাউকে থাকতে দেননি। ব্যালে নর্তকীর মত সেদিকে মুখ করে এক পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য মাটি থেকে উঠলেন, দূর থেকে বোঝার উপায়ও নেই, পা মাটি স্পর্শ করে আছে। বোঝা যেতও না, যদি না প্রবীর ঘোষ থাকতেন। শনিবার আলি ফিরে গেলেন। তার আগে দুপুরে তাঁর কাছে গিয়েছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির প্রবীর ঘোষ, যিনি নিজে ম্যাজিকের ভাণ্ডার এবং যাঁর কাজ অলৌকিক ঘটনার বিজ্ঞানম্মত ব্যাখ্যা দেওয়া। তিনিই ধরলেন ম্যাজিকটা। পরে হোটেলের লাউঞ্জে নিজে করেও দেখালেন। আধ ঘণ্টা আলির সঙ্গে ছিলেন ভদ্রলোক। জমে উঠল দারুণ আড্ডা। দুজনে মেতে উঠলেন ম্যাজিক বিনিময়ে। আলি বের করলেন ম্যাজিক বক্স। দুটো ছোট স্পঞ্জের বল নিয়ে একটা নিজের বাঁ হাতে রেখে অন্যটি দিলেন প্রবীরবাবুর হাতে। কয়েক সেকেণ্ড পর আলি হাত খুললেন, দেখা গেল হাত ফাঁকা। দুটি বলই প্রবীরবাবুর হাতে। প্রবীরবাবু এতো টাকার মুদ্রা ঢুকিয়ে ফেললেন সরু মুখের একটা বোতলের মধ্যে। আবার বের করে আনলেন বোতল ও মুদ্রা অক্ষত রেখে। পরে বিস্মিত আলিকে রহস্যটা ফাঁস করে দিলেন প্রবীর ঘোষ—মুদ্রাটা বিশেষভাবে নির্মিত, ভাঁজ করে সরু করা যায়। আলিকে কয়েকটা উপহার দিলেন। আর্লি আরও অবাক একটা মুদ্রা থেকে দুটো হওয়া দেখে।