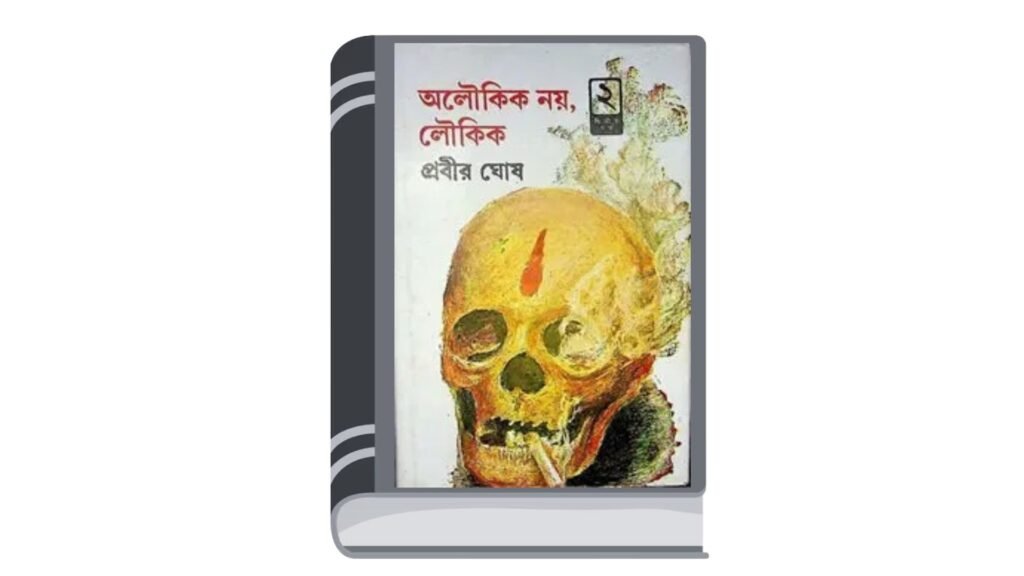অধ্যায় চার: ভূতুড়ে চিকিৎসা
ভূতুড়ে চিকিৎসা
ফিলিপিনো ফেইথ হিলার ও ভূতুড়ে অস্ত্রোপচার
৩১ আগস্ট, ১৯৮৬, রবিবারের সকাল। আর পাঁচটা রবিবারের সকালের মতোই বৈঠকখানায় তখন গাদা গাদা চায়ের কাপ আর রাশি রাশি সিগারেটের ধোঁয়ার মাঝে আড্ডা জমে উঠেছে। এমন সময় আমার ভায়রা সুশোভন রায়চৌধুরী এসে কোনও ভণিতা না করেই একটা দারুণ উত্তেজক খবর দিল—অতি সম্প্রতি ম্যানিলা থেকে একজন অলৌকিক ক্ষমতাবান ডাক্তার এসেছেন কলকাতায়; রোগীকে অজ্ঞান না করে, স্রেফ খালি হাতে, ব্যথাহীন অস্ত্রোপচার করে রোগ সারিয়ে দিচ্ছেন। ওর পরিচিত একজন অস্ত্রোপচার করিয়ে ভালো হয়ে গেছেন। অস্ত্রোপচারের দাগটি পর্যন্ত নেই। খরচ পড়েছে পাঁচ হাজার টাকা। সুশোভনের আমাকে খবরটা দেওয়ার কারণ, যদি এই অলৌকিক রহস্য উন্মোচন করতে পারি।
আমার কাছে কলকাতায় ম্যানিলার অলৌকিক চিকিৎসকের উপস্থিতির খবরটা অবিশ্বাস্য ও অভাবনীয়। সুশোভন যাঁকে অলৌকিক ক্ষমতাবান ডাক্তার বলে অবহিত করল তিনি এবং তাঁর মতো ক্ষমতাবান চিকিৎসকরা নিজেদের পরিচয় দেন ‘ফেইথ হিলার’ বলে। যে ফেইথ হিলারদের নিয়ে পৃথিবী জুড়ে হইচই, তাঁদেরই একজন এই মুহূর্তে কলকাতার বুকে প্রতিদিন বহু রোগীর ওপর অলৌকিক (?) অস্ত্রোপচার করে চলেছেন—কথাগুলো আমি ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারিনি। গোটা ব্যাপারটাই ব্যাণ্ডেজ ভূতের মতোই গুজব নয়তো? খবরটা আমার কাছে অভাবনীয় এই জন্যে, মাত্র সপ্তাহতিনেক আগে আমার কিছু বন্ধুর কাছে বলেছিলাম, ‘ফেইথ হিলারদের হিলিং ব্যাপারটা এখনও কিছুটা রহস্যময় রয়ে গেছে। তাঁদের অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে কৌশলটা ঠিক কী ধরনের এটা এখনও বিজ্ঞানীদের কাছে পরিষ্কার নয়। যদিও James Randi তাঁর ‘Flim-Flam’ বইতে এই বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছেন, তবু তাঁর লেখাতে দুটি দুর্বল দিক রয়েছে। এক: তিনি নিজে ফেইথ হিলারদের মুখোমুখি হননি, দুই: তাঁর বর্ণিত কৌশলের সাহায্যে একজন ফেইথ হিলারের পক্ষে একটা অপারেশন টেবিলে দাঁড়িয়ে অন্যের চোখের সামনে পরপর একাধিক অপারেশন অসম্ভব।
অথচ আমি ম্যানিলা থেকে অলৌকিক অস্ত্রোপচার করিয়ে আসা তিনজনের সঙ্গে কথা বলে যা জেনেছি, তাতে ফেইথ হিলাররা স্থান ত্যাগ না করে অপারেশন টেবিলে এক নাগাড়ে দশ থেকে কুড়ি জনের ওপর অস্ত্রোপচার করেন। যদি কিছু টাকা জোগাড় করতে পারতাম, ফেইথ হিলিং রহস্যভেদের একটা চেষ্টা করতাম, ম্যানিলায় গিয়ে নিজের ওপর ফেইথ হিলিং করিয়ে।”
সেখানে উপস্থিত এক বন্ধু তখনই জানায়, সে আমার ম্যানিলায় যাতায়াতের খরচ বহন করতে রাজি আছে। বাকি ছিল কয়েক দিন হোটেলে থাকা ও ফেইথ হিলিং-এর খরচ বহন করার ব্যাপার। গত তিন সপ্তাহ ধরে টাকা জোগাড় করা এবং ফিলিপিন-এ যাওয়ার প্রাথমিক প্রস্তুতি চলছিল। ঠিক এই সময় কলকাতায় ফেইথ হিলারের উপস্থিতি—এ যেন ‘মেঘ না চাইতেই জল’। খবরটা আমার কাছে অভাবনীয়, অপ্রত্যাশিত এবং উল্লসিত হবার মতো।
সুশোভনকে অনুরোধ করলাম ব্যথাহীন অস্ত্রোপচারে ভালো হওয়া শুর পরিচিত লোকটির কাছ থেকে অলৌকিক ডাক্তারের ঠিকানাটা অবশ্যই এক দিনের মধ্যে জোগাড় করে দিতে।
সুশোভন অবশ্য শেষ পর্যন্ত ঠিকানা দেয়নি, তবে আমারই এক বন্ধু দেবু দাস-এর কাছে ২ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার খবর পেলাম, এর পরিচিত এক তরুণ তমোনাশ দাস ফেইথ হিলারের রিসপেশনিস্ট-এর কাজ করছে।
দেবুর কাছ থেকে ঠিকানা ও একটা পরিচয়পত্র নিয়ে সেই রাতেই তমোনাশের বাড়ি গিয়ে দেখা করলাম। স্মার্ট, ফর্সা, সুদর্শন তরুণ। হোটেল ম্যানেজমেণ্টের পরীক্ষা দিয়ে বসে আছে।
আমি দেবু’র বন্ধু, লেখালেখি করি এবং অলৌকিক বিষয়ে খুবই আগ্রহী জেনে আমার প্রতি যথেষ্ট উৎসাহ দেখালেন তমোনাশ। জানালাম, “গলব্লাডার, হার্ট আর ফ্যারেনজাইটিস নিয়ে জেরবার হয়ে আছি। ফেইথ হিলারের সাহায্য চাই। সেই সঙ্গে এই অলৌকিক চিকিৎসা বিষয়ে পত্রিকায় কিছু লিখতে চাই।”
তমোনাশ জানালেন, কয়েকজন সাংবাদিক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার তরফ থেকে ইতিমধ্যে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তাঁদের প্রত্যেককেই হাত জোড় করে জানিয়েছি ক্ষমা করবেন। আমরা প্রচার চাই না। প্রচার ছাড়াই যে বিপুল সংখ্যাক রোগী আসছেন, তার ভিড় সামাল দিতেই হিমশিম খাচ্ছি, অত এব মাপ করবেন। তবে আপনার চিকিৎসার বিষয়ে নিশ্চয়ই সাহায্য করব। এ জন্য আপনাকে দিতে হবে পাঁচ হাজার টাকা ক্যাশ।”
“যারা চিকিৎসা করাতে আসছেন তাঁরা কেমন ফল পাচ্ছেন?”—জিজ্ঞেস করলাম।
“মিরাকল রেজাল্ট।” কয়েকজন রোগীর নাম ও তাদের আরোগ্যলাভের গল্প বলতে বলতে আমার মতো একজন উৎসাহী শ্রোতাকে দেখাবার জন্য ঘরের ভিতরে গিয়ে নিয়ে এলেন কয়েকটা রঙিন ফটোগ্রাফ। তমোনাশের উপর ফেইথ হিলিং চলাকালীন তোলা ছবি।
বললাম, “আপনার ছবি দিয়ে আপনার ফেইথ হিলিং-এর অভিজ্ঞতার কথাই পাঠকদের কাছে তুলে ধরতে চাই।”
আমার কথায় চিঁড়ে ভিজল মনে হল। খাতা-কলম বের করে তমোনাশের অভিজ্ঞতার কথা জেনে টুকে নিতে শুরু করলাম।
ফিলিপিন থেকে আসা এই ফেইথ হিলারের নাম Mr. Romeo P. Gallarrdo। সহকারী হিসেবে সঙ্গে এসেছেন Mr. Rosita J. Gallardo| উঠেছেন কলকাতার লিটন হোটেলে। এঁদের ভারতে নিয়ে আসার আর্থিক দায়-দায়িত্ব নিয়েছেন গৌহাটির কোটিপতি ব্যবসায়ী রামচন্দ্র আগরওয়াল। কলকাতার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়েছেন রামচন্দ্র আগরওয়ালের শ্যালক অলোক খৈতান। শারীরিক ও মানসিকভাবে আরও বেশি রকম সুস্থ ও চনমনে হতে গ্যালার্ডোর ফেইথ হিলিং-এর সাহায্য নিয়েছিলেন তমোনাশ। দারুণ কাজ হয়েছে। তমোনাশকে এ জন্য কোনও টাকা দিতে হয়নি। মিস্টার গ্যালার্ডোর সঙ্গে তমোনাশের খুব ভালো ভাব হয়ে গেছে। ভিড় ভালোই হচ্ছে। দিনে রোগী আসছেন একশো থেকে দেড়শো।
তমোনাশের ছবিগুলো থেকে দুটো ছবি নিয়ে বললাম, “এই ছবি দুটো সহ লেখাটা ছাপতে চাই। লেখাটা আরও ভালো হত যদি গ্যালার্ডোর একটা সাক্ষাৎকার সঙ্গে ছাপতে পারতাম।”
তমোনাশ বললেন, “কাল রাতে একবার আসুন। আমি গ্যালার্ডোর সঙ্গে কথা বলে দেখি কিছু করা যায় কি না।”
তিন তারিখ রাতে খবর পেলাম, মিস্টার গ্যালার্ডো জানিয়েছেন মিস্টার আগরওয়ালের অনুমতি ছাড়া তাঁর পক্ষে কোনও সাক্ষাৎকার দেওয়া সম্ভব নয়। তমোনাশ মিস্টার আগরওয়ালের সঙ্গেও কথা বলেছিলেন। আগরওয়াল আমার বিষয়ে অনেক কিছুই জানতে চেয়েছিলেন। কাজ উদ্ধার করতে সত্যি-মিথ্যে কল্পনা সব মিশিয়ে যা হোক উত্তর খাড়া করে দিয়েছেন তমোনাশ। মিস্টার আগরওয়াল কাল তাঁর মতামত জানাবেন বলেছেন। চার তারিখ রাতে আবার গেলাম। খবর পেলাম, গ্যালার্ডোর সাক্ষাৎকার পাওয়ার অনুমতি মিলেছে। ছয় সেপ্টেম্বর শনিবার ২-৩০ মিনিটে লিটন হোটেলের ৪৬ নম্বর রুমে দেখা করতে বললেন তমোনাশ। ওই রুমেই ‘আপাতত আগরওয়াল, খৈতান ও তমোনাশের আস্তানা। সেদিনই সাক্ষাৎকারের পরে আমার চিকিৎসাও করা হবে।
’৮৫-র এপ্রিলে ইংলণ্ডের গ্রানেডা টেলিভিশন প্রোডাকশনের একটা তথ্যচিত্রের ভিডিও দেখি। নাম ছিল ‘World in Action’। ছবিটি ফিলিপিনের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাবান চিকিৎসক ফেইথ হিলারদের নিয়ে তোলা। ফেইথ হিলাররা যে কোনও রোগেরই চিকিৎসাক করেন তাঁদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতার দ্বারা। চিকিৎসা পদ্ধতিও বিচিত্র। রোগীকে অপারেশন টেবিলে শুইয়ে দেওয়া হয়। ফেইথ হিলার বিড়বিড় করে ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করেন। তারপর শরীরের যে অংশে অস্ত্রোপচার করবেন, সেখানে দু-হাতে সামান্য জল ও এক ধরনের তৈলাক্ত পদার্থ ছিটিয়ে সামান্য মালিশ করেন। এবার শুরু হয় অস্ত্রহীন অস্ত্রোপচার। ফেইথ হিলার নিজের হাতের আঙুলগুলো রোগীর শরীরের যে অংশে অস্ত্রোপচার করা হবে সেই অংশে ঢুকিয়ে দিতে থাকেন। বেরিয়ে আসতে থাকে তাজা লাল রক্ত। ফিলিপিনো ফেইথ হিলারদের ভাষায় এগুলো ‘Devil Blood’ বা ‘শয়তানের রক্ত’।
হার্ট, লাংস, কিডনি, অ্যাপেনডিকস, টিউমার, গলব্লাডার প্রভৃতি বড়বড় অপারেশনও ফেইথ হিলাররা করে থাকেন। এইসব অপারেশনও করা হয় একইভাবে, রোগীকে অজ্ঞান না করে কোনও অস্ত্রের সাহায্য ছাড়া এবং অবশ্যই ব্যথাহীন ভাবে পাঠকদের মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগছে, তবে কি এঁরা হাতের নখের সাহায্য নেন? না, তাও নয়, নখ নিখুঁত ছাঁটা। স্রেফ দু-হাতের বা এক হাতের আঙুলের সাহায্যেই ওঁরা রোগীর শরীর কাটা-ছেঁড়ার কাজ করেন। হাত তুললেই শুধু রক্ত। ফেইথ হিলারের সহকারী তুলো দিয়ে রক্ত মুছে নিতেই দেখা যায় অস্ত্রোপচারের কোনও চিহ্ন নেই, আপনা থেকেই কাটা জায়গা জোড়া লেগে গেছে। যত বড়ই অস্ত্রোপচার হোক না কেন, রোগীকে একটুও ব্যথায় কাতর হতে দেখা যায় না। ফেইথ হিলিং চিকিৎসার সাহায্য নেওয়ার পর অনেকেরই বক্তব্য— তাঁরা ভালো আছেন।
‘ওয়ার্ল্ড ইন অ্যাকশন’ ছবিতে গ্রানাডা টিভি প্রোডাকশনের ভাষ্যকার বা narrator ছিলেন মাইক স্কট। টিভির সামনে একজন ফেইথ হিলার একটি বালিকার গলা থেকে একটা ‘গ্রোথ’ (growth) অস্ত্রোপচার করলেন স্রেফ খালি হাতে। এক্ষেত্রেও অজ্ঞান না করে ব্যথাহীন অস্ত্রোপচার। অস্ত্রোপচার শেষ হতেই মাইক স্কটের সহকর্মীরা ওই গ্রোথটি এবং রক্তাক্ত তুলো সংগ্রহ করেছিলেন।
ফেইথ হিলার Jose Mercado এবার যার উপর অস্ত্রোপচার করলেন তিনি বেশ মোটাসোটা মানুষ। পেটে নাকি টিউমার। কিছুটা তেল আর জল পেটে ছড়িয়ে কিছুক্ষণ ধরে মালিশ ও প্রার্থনা চলল। একসময় “রোগীর পেটের উপর মার্কাডো নিজের হাত দুটো পাশাপাশি রাখলেন। তারপর মুহূর্তে বাঁ হাত দিয়ে পেটে চাপ দিয়ে ডান হাতটা ঢুকিয়ে দিলেন রোগীর পেটে। বেরিয়ে এল রক্ত। সহকারী তুলো দিয়ে রক্তগুলো মুছতে লাগলেন। মার্কাডো পেট থেকে হাত বের করলেন। হাতে ধরা রয়েছে টিউমার। সহকারী রক্তধারা মুছিয়ে দিতেই কোন্ জাদুবলে অস্ত্রোপচারের চিহ্ন অদৃশ্য হল। পেট দেখলে বোঝার উপায় নেই কখনও এখানে অস্ত্রোপচার হয়েছিল।”


দূরদর্শনের ভাষ্যকার স্কট অতি তৎপরতার সঙ্গে টিউমারটি মার্কাডোর হাত থেকে তুলে নিলেন, সেই সঙ্গে কিছুটা রক্তাক্ত তুলো।
মেয়েটির গ্রোথ এবং রক্তাক্ত তুলো পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয় Guy’s Hospital London-এর ডিপার্টমেণ্ট অফ ফরেনসিক মেডিসিনে। মেয়েটির গলার গ্রোথ বায়পসি করে জানা যায় দেহাংশটি একটি পূর্ণবয়স্ক যুবতীর স্তনের অংশ ও রক্তের নমুনা মানুষের নয়।
পুরুষ মানুষটির টিউমার ও রক্তাক্ত তুলো পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল লণ্ডন হসপিটাল মেডিকেল কলেজের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার PJ. Lincoln-এর কাছে। পরীক্ষার পর লিংকন মত দেন তথাকথিত টিউমারটি আসলে মুরগির দেহাংশ এবং রক্তের নমুনা গরুর।
দেহাংশ ও রক্ত নমুনার পরীক্ষার ফল স্পষ্টতই বুঝিয়ে দেয় এগুলো রোগিণী ও রোগীর দেহাংশ বা রক্ত আদৌ নয়। অর্থাৎ রোগীর দেহে কোনও অস্ত্রোপচারই করা হয়নি এবং অস্ত্রোপচার করে বার করে আনা হয়নি কোনও দেহাংশ। তবে এতগুলো অনুসন্ধিৎসু চোখ ও টি ভি ক্যামেরা যা দেখল সেটা কী? রোগীরা যা অনুভব করলেন তার কি কোনোই গুরুত্ব নেই?
এ ক্ষেত্রে অবশ্য নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় না—ফেইথ হিলার প্রতারক। কারণ, পরীক্ষা গ্রহণকারীদের পক্ষে দেহাংশ ও রক্তের নমুনা পাল্টে দেবার সুযোগ ছিল। যেহেতু সরকারিভাবে কোনও ফরেনসিক বিভাগ অস্ত্রোপচারের সঙ্গে সঙ্গে দেহাংশ ও রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে তা সিল করে পরীক্ষার দায়িত্বগ্রহণ করেনি, তাই সুনিশ্চিতভাবে কোনও কিছুই প্রমাণিত হয় না।
ফেইথ হিলারদের কাছে যে সব রোগী চিকিৎসা করিয়েছেন তাঁদের কিছু ঠিকানা জোগাড় করে গ্রানেডা টিভি প্রোডাকশন। কেইথ হিলিং-এর পর বর্তমানে তাঁরা কেমন আছেন, এই তথ্য সংগ্রহই ছিল গ্রানেডার উদ্দেশ্য। ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। যাঁদের মতামত সংগ্রহ করা গিয়েছিল তাঁদের বেশির ভাগই জানান, ফেইথ হিলিং-এরপর অনেকটা সুস্থ, অনুভব করেছিলেন, কিন্তু বর্তমানে আবার উপসর্গগুলো ফিরে এসেছে। বাকি রোগীরা জানান—এখন সামান্য ভালো অনুভব করছেন (‘felt a little better’)|
দুই ফেইথ হিলার David Elizalde এবং Helen Elizalde-এর অলৌকিক অস্ত্রোপচারের উপর B.B.C. একটা অনুষ্ঠান প্রচার করে। অনুষ্ঠানটির পরিচালক ডেভিড ও হেলেনকে জালিয়াত, ধোঁকাবাজ এবং প্রতারক বলে বর্ণনা করেন। কারণ, মানুষের দেহে অস্ত্রোপচার করে তাঁরা যা বের করেছিলেন, পরীক্ষার ফলে তা শুয়োরের দেহাংশ বলে B.B.C. জানান। এই ক্ষেত্রেও রক্তের নমুনা পরীক্ষা করে জানা যায়—মানুষের রক্ত নয়। এ ক্ষেত্রেও নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়নি সংগৃহীত নমুনাই পরীক্ষিত হয়েছিল। কারণ এটাও আগের মতোই সরকারি পরীক্ষা ছিল না। ছিল সম্পূর্ণ বে-সরকারি উদ্যোগে পরীক্ষা।
ফেইথ হিলিং ব্যাপারটার মধ্যে একটা ধোঁকাবাজি আছে এ কথা একাধিকবার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি প্রমাণ করার চেষ্টা করলেও ওঁরা কী কৌশলে নিজেদের হাতের আঙুলগুলো রোগীর শরীরে ঢুকিয়ে দেন এবং কী কৌশলেই বা তৎক্ষণাৎ রক্তের আমদানি করেন, কেমন করেই বা আসে অস্ত্রোপচারে বিচ্ছিন্ন করা দেহাংশ, এসব প্রশ্নের উত্তর কিন্তু কেউই যুক্তিপূর্ণভাবে হাজির করতে পারেননি।
ফেইথ হিলারদের ফেইথ হিলিং-এর কৌশলগত দিক নিয়ে আলোচনা করে যিনি যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করতে পেরেছেন তিনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তিবাদী বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব James Randi। তিনি তাঁর ‘FLIM FLAM’ বইতে একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, ফেইথ হিলাররা অস্ত্রোপচারের আগে নিজের বুড়ো আঙুলে একটা নকল বুড়ো আঙুলের খাপ পরে নেয়া নকল আঙুলের খাপে লুকোনো থাকে রক্ত এবং ফেইথ হিলারের সহকারীর তুলোয় জড়ানো থাকে মাংস।
র্যাণ্ডির লেখাটা পড়ে আমার মনে হয়েছিল ফেইথ হিলিং-এর গোপন কৌশল বলে তিনি যা বর্ণনা করেছেন তাতে কিছু ফাঁক-ফোকর রয়েছে। এক: এভাবে দর্শকদের সামনে পরপর একাধিক রোগীর ওপর অস্ত্রোপচার করা অসম্ভব। কারণ বুড়ো আঙুলের খাপে লুকিয়ে রাখা রক্তের পরিমাণ অতি সীমিত হতে বাধ্য। দুই: টিভি ক্যামেরার ক্লোজ-আপ এবং হাত দুয়েক দুরে দাঁড়িয়ে থাকা পরীক্ষক বা দর্শকদের নকল আঙুলের সাহায্যে ঠকানো খুব একটা সহজসাধ্য বলে মনে হয় না।
জেমস র্যাণ্ডির অবশ্য এই বিষয়ে কিছু ভ্রান্তি হতেই পারে, কারণ তিনি নিজে ফেইথ হিলারদের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ পাননি। র্যাণ্ডি ফিলিপাইনে গিয়ে কেইথ হিলারদের উপর অনুসন্ধান চালাতে চেয়ে ফিলিপাইন সরকারের কাছে ভিসা প্রার্থনা করেন। ফেইথ হিলারদের উপর অনুসন্ধানের নামে তাঁদের কোনও রকমে অসম্মান জানালে ফিলপাইনবাসীদের কাছে তা ধর্মীয় আঘাত বলে বিবেচিত হতে পারে, এই অজুহাতে ফিলিপাইন সরকার জেমস র্যাণ্ডিকে ভিসা দেননি বলে র্যাণ্ডি স্বয়ং অভিযোগ তুলেছেন।
ফেইথ হিলারদের অলৌকিক ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সে সব বই আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে বিশ্বের জনপ্রিয়তম বইটি সম্ভবত ‘Arigo: Surgeon of the Rusty Knife’। লেখক John Fuller। Arigo ছদ্মনামের আড়ালে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাবান ফেইথ হিলারটির নাম Jose Pedro de Feitas।
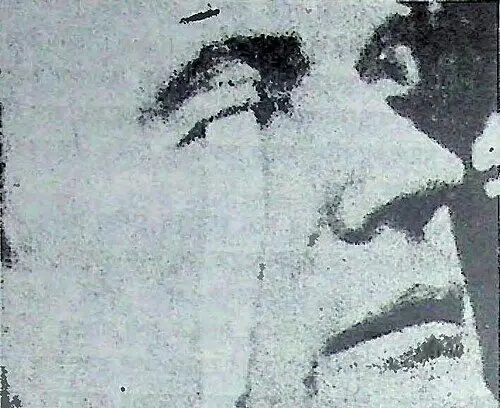
অ্যারিগো আর দশজন ফেইথ হিলারের মতোই সাদা পোশাক পরে গ্লাভস ছাড়াই রোগীদের উপর খালি হাতে দ্রুত অস্ত্রোপচার করেন, তবে অস্ত্রোপচারের আগে একটা ছুরির বাঁট দিয়ে রোগীর চামড়াটাকে একটু ঘষে নেন। অস্ত্রোপচার শেষে সেলাই না করেই একটু হাত ঘষে কাটাটা আবার জুড়ে দেন। তারপর অতি-জড়ানো হাতের লেখায় যে প্রেসক্রিপশন লেখেন, সেটি নাকি তিনি তাঁর নিজের বিবেচনামাফিক লেখেন না। এক মৃত জার্মান
অ্যারিগোডাক্তার Dr. Fritz-এর আত্মা নাকি অ্যারিগোর বাঁ কানে ফিসফিস করে যে ওষুধের কথা বলেন অ্যারিগো তাই লেখেন।
অ্যারিগোর প্রেসক্রিপশনের লেখা এতই জড়ানো যে শহরের একটি মাত্র ফার্মেসিই সেই লেখা পাঠোদ্ধার করতে পারে। ফার্মেসির মালিক অ্যারিগোর ভাই।
জন ফাউলার তাঁর বইটির তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত ধনকুবের বিজ্ঞানী ও অলৌকিকবাদের ধারক-বাহক ড. আণ্ড্রুজা পুহারিক প্রযোজিত অ্যারিগোর ওপর তোলা একটি ফিল্ম দেখে।
অ্যারিগোর ফেইথ হিলিং ছাড়া আর যে ‘impossiblities’ দেখে ড. পুহারিক বিহ্বল হয়েছিলেন তা হল অ্যারিগোর একটি মুদ্রাদোষ। অ্যারিগো কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝেই নিজের চোখে ছুরি ঢুকিয়ে দেন, যেটা ড. পুহারিকের মতে কোনও মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। এ এক অলৌকিক ক্ষমতারই প্রকাশ।
ড. পুহারিকের এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ইতালির Piero Angela এক পদ্ধতিতে বারবার চোখে ছুরি ঢুকিয়ে প্রমাণ করেছেন, এই ধরনের কোনও কিছু ঘটালে সেটা অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার সাক্ষ্য বহন করেন না। এটা একটা কষ্টসাধ্য অনুশীলনের ফল মাত্র।
আর যাই হোক, এটা কিন্তু স্বীকার করতেই হবে ‘ফেইথ হিলার’ নাম অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাবান (?) কিছু চিকিৎসক তাঁদের অদ্ভুত চিকিৎসা পদ্ধতির দ্বারা পৃথিবীর প্রতিটি উন্নত দেশে প্রচণ্ড রকমের হইচই ফেলে দিয়েছেন। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষা-ভাষী পত্রিকায় এঁদের নিয়ে লেখা হয়েছে এবং হচ্ছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ব্রিটেন ও ইতালির মানুষ তাঁদের দেশের টিভিতে ফেইথ হিলারদের অলৌকিক কার্যকলাপ দেখে শিহরিত হয়েছেন, এই তথাটা আমার জানা। জানি না আরও কতগুলো দেশ ফেইথ হিলারকে টিভি ক্যামেরায় বন্দি করেছে।
সম্পূর্ণ কষ্টহীন ও ঝুঁকিহীন ভাবে আরোগ্যলাভের আশায় প্রতি বছর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জাপান এবং ইউরোপ ও আরবের বিভিন্ন দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ নানা রকমের দুরারোগ্য রোগ সারাতে ম্যানিলায় যান। এইসব দেশের মতো এত বিশাল সংখ্যা না হলেও ভারতবর্ষ থেকে, এমনকী, আমাদের কলকাতা শহর থেকেই প্রতি বছর কিছু লোক চিকিৎসিত হতে ম্যানিলায় যান। এই লক্ষ লক্ষ আরোগ্যকামী বিদেশিদের কল্যাণে ম্যানিলায় গড়ে উঠেছে জমজমাট হোটেল ব্যবসা। আমদানি হচ্ছে মূল্যবান বিদেশি মুদ্রা।
চিকিৎসার জন্য কোনও অর্থ গ্রহণ করেন না ফেইথ হিলাররা। শুধু নাম তালিকাভুক্ত করার সময় ’৮৬-তে ভারতীয় টাকায় আড়াইশো টাকার মতো জমা দিতে হত। সাধারণভাবে চিকিৎসা চলে রোগের গুরুত্ব অনুসারে তিন থেকে সাত দিন। প্রতিদিনই রোগীর দূষিত রক্ত শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে বের করে দেন ফেইথ হিলার। চিকিৎসা শেষে রোগীর কাছে দেশের গরিবদের সাহায্যার্থে সাধারণত ৫০০ ডলার সাহায্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়।
ফিলিপাইনস্ ফেইথ হিলারদের লীলাক্ষেত্র হলেও, এরা মাঝে-মধ্যে অন্য কোনও দেশের ধনকুবেরের সঙ্গে আর্থিক চুক্তি করে সেই দেশে দু-এক মাসের জন্য পাড়ি দেন অলৌকিক চিকিৎসার পসরা নিয়ে।
তেমন রমরমা প্রতিষ্ঠা না পেলেও, ব্রাজিল এবং পেরুর কয়েকজন আধ্যাত্মিক নেতা অলৌকিক ক্ষমতা পেয়ে ফেইথ হিলিং শুরু করেছেন। পাঁচ সেপ্টেম্বর সকাল থেকেই ‘ভারতীয় যুক্তিবাদী সমিতি’র (বর্তমান নাম—ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি) কয়েকজন সদস্য পালা করে হোটেল লিটনের উপর নজর রাখতে লাগলেন। সন্ধের মধ্যে খবর পেলাম ওই ৪৬ নম্বর ঘরে অসম, অ.গ.প.-র জনৈক নেতাও নাকি প্রায় পুরো সময়ই ছিলেন। মিস্টার ও মিসেস গ্যালার্ডো আছেন ৪৪ নম্বর ঘরে। এছাড়া আর এমন কিছু খবর পেলাম যার ফল এটুকু বুঝতে অসুবিধে হল না যে আমাকে অস্ত্রোপচার করার পর সেই রক্তের নমুনা সংগ্রহ করার চেষ্টা করাটা অত্যধিক ঝুঁকির ব্যাপারে হবে। কথাটা বোধহয় ভুল বললাম। বরং সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে আমরা বিশ্বাস করেছিলাম ওদের বিরুদ্ধে, কিছু করতে গেলে হোটেল লিটনের বাইরে আমাদের জীবিত দেহ আর কোনো দিনই বের হবে না। ছয় তারিখ বারোটা থেকে আমি লিটন থেকে না বের হওয়া পর্যন্ত আর কয়েকজন অতিরিক্ত যুক্তিবাদী সদস্যকে লিটনে নজর রাখার জন্য নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। এঁরা কেউই বিপদে খুব একটা ঘাবড়ে যাওয়ার মতো নন।
সেদিন দুপুর সাড়ে এগারোটায় ফোন করলাম কলকাতা পুলিশের তৎকালীন যুগ্ম-কমিশনার সুবিমল দাশগুপ্তকে। ফেইথ হিলারদের রহস্যময় চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে বলে জানালাম, বর্তমানে আমাদের এই শহরের লিটন হোটেলে বিশ্বখ্যাত এক ফেইথ হিলার অবস্থান করছেন। আজ আড়াইটের সময় আমি তাঁর একটা সাক্ষাৎকার নেব, তারপর আমার উপর অপারেশন করাব। ইনিই সম্ভবত প্রথম ফিলিপিনো ফেইথ হিলার যিনি ভারতে এলেন।
সুবিমলবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “এই বিষয়ে তোমার মত কী? সত্যিই কি ওঁরা খালি হাতে অপারেশন করেন?”
বললাম, “আমার ধারণা পুরোটাই একটা বিশাল ধাপ্পা। আমি আশা রাখি ওদের কৌশলটা ধরতে পারব। এই বিষয়ে আপনার একটু সাহায্য চাই বলেই ফোন করা। আমাকে অপারেশন করার পর আমার শরীর থেকে যে রক্ত বের হবে তার নমুনা আপনি ফরেনসিক টেস্টের জন্য সংগ্রহ করলে বাধিত হব। কারণ এই রিপোর্টই পারে ওই দীর্ঘদিনের এক সন্দেহের ও বিতর্কের অবসান ঘটাতে।”
ও প্রান্ত থেকে উত্তর এল, “মোস্ট ইণ্টারেস্টিং। নিশ্চয়ই যাব। কটায় তোমার অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট?”
“দুটো তিরিশে, হোটেল লিটনে। একটি অনুরোধ, প্লেন ড্রেসে যাবেন।”
“তুমি ঠিক দুটোয় লালবাজারে চলে এসো॥”
আড়াইটের আগেই হোটেল লিটনে পৌঁছলাম। সুবিমলবাবুর সরকারি অ্যামবাসেডার আর দেহরক্ষীদের আমরা ত্যাগ করলাম। গ্লোব সিনেমা হলের কাছে। হোটেলে ঢুকলাম আমরা পাঁচজন। আমি, সুবিমল দাশগুপ্ত, ভারতীয় যুক্তিবাদী সমিতির দুই সভ্য প্রাক্তন টেবিল টেনিস খেলোয়াড় জ্ঞান মল্লিক, চিত্র-সাংবাদিক সৌগত রায়বর্মন এবং দর্শক হিসেবে আমার অফিসের এক সহকর্মী।
প্রথম হানা দিলাম ৪৪ নম্বরে ঘরে। নক্ করতেই দরজা খুললেন মিস্টার গ্যালার্ডো। পরিচয় দিয়ে কথা বলতে চাইলাম। ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে মিস্টার গ্যালার্ডো জানালেন,
“আপনার কথা মিস্টার তমোনাশের কাছে শুনেছি। আপনি আসায় খুশি হয়েছি, দয়া করে ৪৬ নম্বর রুমে মিস্টার আগরওয়ালের সঙ্গে আগে দেখা করুন। একটু পরেই আমি আসছি। মিস্টার আগরওয়ালের সামনে ছাড়া আমি কোনও ইণ্টারভিউ দিতে অক্ষম।”
৪৬ নম্বর রুমে অনেককেই পেলাম। রামচন্দ্র আগরওয়াল, অলোক খৈতান, তমোনাশ দাস এবং অসম অগ.প. নেতা বলে পরিচয় দেওয়া জনৈক বসন্ত শর্মাকে। তমোনাশই ওঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।
আমার চার সঙ্গীর সঙ্গে ওঁদের পরিচয় করিয়ে দিলাম। শুধু সুবিমল দাশগুপ্তের বেলায় মিথ্যে বললাম, “মিস্টার দাশগুপ্ত, আমার কাজিন ব্রাদার।” আমরা সকলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে খুব দ্রুত খোলামেলা আলোচনায় মেতে উঠলাম। আগরওয়াল এবং অলোক খৈতান দুজনেই ভালোই বাংলা বলেন।
একসময় আমার প্রশ্নের উত্তরে মিস্টার আগরওয়াল জানালেন, “আমার এক আত্মীয়ের একটা চোখ অন্ধ হয়ে যায়। ম্যানিলায় গিয়ে ফেইথ হিলিং করিয়ে সে আবার দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে। তখনই আমার মাথায় একটা চিন্তা ঢোকে। বড়লোকেরা না হয় রোগ সারাতে ম্যানিলায় যেতে পারে, কিন্তু গরিবদের কঠিন অসুখ হলে তারা কী করবে? ভাবলাম দেশের সাধারণ মানুষদের জন্য না হয় কিছু খরচা করলামই। আমার আত্মীয়ের কাছ থেকে ডাক্তারের ঠিকানা নিয়ে ‘ফেইথ হিলিং করতে যাচ্ছি’ জানিয়ে ভিসা করে ম্যানিলায় চলে গেলাম। ওখানে মিস্টার গ্যালার্ডোর সঙ্গে দেখা করে আমার পরিকল্পনা জানাই। উনি খুবই ভালো লোক, আধ্যাত্মিক জগতের লোক তো আমার কথায় ভারতে আসতে রাজি হলেন।
“৭ আগস্ট মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস গ্যালার্ডো কলকাতায় আসেন। এই হোটেলেই ওঠেন। আমাদের চেনা-শোনা ও পরিচিতদের মধ্যে অনেকেই ফেইথ হিলিং-এর সুযোগ নিতে শুরু করেন। এখানে বারো দিন থাকার পর ২০ আগস্ট আমি আর অশোক ওঁদের নিয়ে গৌহাটি যাই। ওখানে ওঁরা পাঁচ দিন ছিলেন। এত ভিড় হচ্ছিল যে, নাওয়া-খাওয়ার সময়টুকু পর্যন্ত পাচ্ছিলাম না। একদিন তো ২০০ রোগী নাম লিখিয়ে ছিলেন। টাকা রোজগারের ধান্দা থাকলে নিশ্চয়ই খুশি হতাম। তা যখন নয় তখন নিজেদের জান বাঁচাতে পালিয়ে এলাম। ২৭ তারিখ থেকে আবার কলকাতায়। ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এখানে থাকার পরিকল্পনা রয়েছে। তারপর হয় তো ওঁদের নিয়ে দিল্লি যেতে পারি।”

আগরওয়াল এই কথার মধ্য দিয়ে বোঝাতে চাইলেন মিস্টার গ্যালাডোকে এদেশে নিয়ে আসার উদ্দেশ্য টাকা রোজগার নয়, নেহাৎই সেবা। তাই আসামের বিশাল টাকার হাতছানিও তিনি অক্লেশে ছেড়ে আসতে পেরেছেন। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস গ্যালার্ডোকে ১৮।৮।৮৬-তে ইস্যু করা পারমিটের একটি প্রতিলিপি আমার হাতে এসেছে যাতে দেখেছি তাদের ২০ আগস্ট-৮৬ থেকে ২৭ আগস্ট ’৮৬ পর্যন্ত আসামে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অতএব রোজগারের ধান্দা থাকলেও ২৭ আগস্টের পর মিস্টার ও মিসেস গ্যালার্ডোর আসামে থাকা সম্ভব ছিল না। আগরওয়ালকে প্রশ্ন করলাম, “আপনি একটু আগে বলছিলেন দেশের গরিব মানুষদের সেবার জন্য মিস্টার গ্যালার্ডোকে নিয়ে এসেছেন। তবে রোগীদের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা করে নিচ্ছেন কেন?”
আমার প্রশ্নের শুনে প্রথমটায় আগরওয়াল সামান্য গুটিয়ে গিয়ে পরে সামলে নিয়ে বললেন, “যে বিশাল খরচ করে এঁদের এনেছি তাতে খরচের কিছুটা অংশ না তুলতে পারলে তো মরে যাব দাদা। হোটেল খরচই মেটাচ্ছি রোজ আট-হাজার টাকা। তার উপর এই হোটেলের মালিকের পাঠানো দুজন করে রোগী প্রতিদিন বিনে পয়সায় দেখে দিচ্ছি।”
হাসলাম, বললাম, “আপনি তো প্রত্যেক রোগীকে দিয়েই একটা ডিক্লেয়ারেশন ফর্ম ফিল-আপ করাচ্ছেন। আমাকে ফর্মের ফাইলটা একটু দেবেন। কিছু রোগীর ঠিকানা নেব। একটা সার্ভে করে দেখতে চাই তাঁরা ফেইথ হিলিং করিয়ে কেমন ফল পেয়েছেন।”
অলোক দু-কাঁধ ঝাঁকিয়ে জানালেন, “ফাইলটা কালই হারিয়ে গেছে।”
কথায় কথায় মিনিট কুড়ি বোধহয় পার হয়েছে, একজন তরুণ ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে তমোনাশকে ইশারায় ডেকে বেরিয়ে গেলেন। তমোনাশও বেরোলেন। মিনিট দুয়েক পরেই তমোনাশ ডাকলেন আগরওয়ালকে। তার মিনিট দুয়েক পরেই আগরওয়াল আমাকে বাইরে ডাকলেন। বাইরে এসে দেখি করিডরে তমোনাশ, আগরওয়াল ও যে ছেলেটি দরজা নক করেছিল সে দাঁড়িয়ে। প্রত্যেকেই যেন কিছুটা অস্বস্তি ও চিন্তার মধ্যে রয়েছেন।
আগরওয়াল আমাকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন, “আপনার সঙ্গে কি সাদা পোশাকে পুলিশ কমিশনার বা জয়েণ্ট কমিশনার রয়েছেন?”
“কেন বলুন তো?”
“না, খবর পেলাম কি, গ্লোব হলের কাছে ওই জাতীয় পদের কারও একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ইউনিফর্ম পরা বডিগার্ড গাড়িতেই রয়েছে। কমিশনার বা জয়েণ্ট কমিশনার যিনিই এসে থাকুন তিনি যখন বডিগার্ড সঙ্গে নেননি তখন প্লেন ড্রেসেই কাছাকাছি কোথাও আছেন। আমাদের মনে হচ্ছে তিনি আপনার সঙ্গে আছেন।”
“হ্যাঁ, মিস্টার দাশগুপ্তের সঙ্গে যে আলাপ করিয়ে দিলাম, তিনিই জয়েণ্ট কমিশনার। তবে আপনার কোনও চিন্তার কারণ নেই। উনিও আমার মতোই ফেইথ হিলারদের অলৌকিক ক্ষমতার বিষয়ে জানতে ও দেখতে উৎসাহী। আমি আজ ইণ্টারভিউ নেব এবং অপারেশন করাব শুনে সঙ্গী হয়েছেন।” ইনফরমার ছেলেটি বিদায় নিল। আমি, আগরওয়াল ও তমোনাশ ঘরে ঢুকলাম। যে ঘটনাটা একটু আগে ঘটল সেটা সবার সামনে বলে পরিবেশটাকে হালকা করতে চাইলাম।
সুবিমলবাবুও হাসতে হাসতে আগরওয়ালকে বললেন, “আমি কিন্তু এখানে এসেছি পৃথিবী বিখ্যাত ফেইথ হিলিং নিজের চোখে দেখব বলে। পুলিশের তকমা এঁটে কারও মনে অস্বস্তি সৃষ্টি করতে চাই না বলেই এই পোশাকে আসা। সুযোগ পেলে আমার কপালের একটা ব্যথা আপনাদের হিলিং-এ সারে কি না একটু পরীক্ষা করে দেখতে পারি।”
এরপর আমাদের আগের মতো খোলামেলা কথাবার্তা আর জমল না। মিনিটদশেক পরে দরজা খুলে মিস্টার ও মিসেস গ্যালার্ডো আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন, “আসুন।”
আমরা হোটেলের কনফারেন্স রুমে এলাম। রুমের একপাশে একটা লম্বা টেবিল প্লাস্টিকের নীল চাদর বিছানো। টেবিলের কাছে দাঁড়ালেন মিস্টার গ্যালার্ডো, পাশে মিসেস। করমর্দন করে দুজনকে শুভেচ্ছা জানালাম। দেখলাম মিস্টার গ্যালার্ডোর প্রতিটি আঙুলের নখই নিখুঁত কাটা।
আমার প্রথম প্রশ্নটা ছিল, “ফেইথ হিলিং-এর সাহায্যে যে কোনও রোগীকে কি রোগমুক্ত করা সম্ভব?”
“হ্যা, নিশ্চয়ই,” গ্যালার্ডো উত্তর দিলেন।
“প্রতিটি ফেইথ হিলিং-এর ক্ষেত্রেই কি অপারেশন করার প্রয়োজন হয়?”
“না, না। শরীরের ভিতর থেকে কোনও দেহাংশ বিচ্ছিন্ন করে বের করতে হলেই শুধু ‘ওপন’ করার প্রয়োজন হয়। অবশ্য হিলিং করার সময় যে কোনও রোগের ক্ষেত্রেই রোগীর শরীর থেকে ‘ডেভিল ব্লাড’ বের করে দিই। সেটাকেও যদি অপারেশন বলতে চান, তো বলতে পারেন।”
“একজন রোগীকে হিলিং করতে কত সময় লাগে?”
“দেড় থেকে তিন মিনিট।”
“আপনি এই ফেইথ হিলিং কোথা থেকে শিখলেন?”
আমার প্রশ্ন শুনে হাসলেন মিস্টার গ্যালার্ডো। বললেন, “এ তো শেখা যায় না। আর আমিও তো চিকিৎসা করি না। ‘গডই রোগীদের চিকিৎসা করেন। আমি গড়ের হাতের যন্ত্র মাত্র। ঈশ্বর যাঁদের মাধ্যমে রোগীদের নিরাময় করান তাদের নির্বাচন করেন তিনি নিজেই।”
“যাঁরা আপনার কাছে আরোগ্যের আশায় আসেন, তাঁরা সকলেই কি রোগ মুক্ত হন?”
“সারবেই, এমন গ্যারাণ্টি আমি কাউকেই দিচ্ছি না। আরোগ্য নির্ভর করে রোগীদের ওপরে। রোগীর যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকে, যদি ফেইথ হিলিং-এ বিশ্বাস থাকে এবং এক মনে ঈশ্বরের কাছে নিজের আরোগ্য কামনা করে তবে নিশ্চয়ই সারবে। তবে এটা কয়েকদিনে সারবে, কি কয়েক সপ্তাহে অথবা কয়েক মাসে, তা সম্পূর্ণই নির্ভর করে রোগীর বিশ্বাস ও প্রার্থনার ওপর।”
মিসেস গ্যালার্ডোকে এবার প্রশ্ন করলাম, “আপনিও ফেইথ হিলার?”
মিসেস গ্যালার্ডো দু’পাশে মাথা ঝাঁকালেন, “না, না, আমি ঈশ্বরের সেই কৃপা পাইনি। স্বামীকে সাহায্য করি মাত্র।”
মিস্টার গ্যালার্ডোকে এবার প্রশ্ন করলাম, “আপনি নিশ্চয়ই পৃথিবীর অনেক দেশ ঘুরেছেন?”
“হ্যাঁ।”
“বিদেশে কোথাও কি কোনও বিজ্ঞান-সংস্থা, বিজ্ঞানী বা চিকিৎসক আপনার চিকিৎসা পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক ব্যাখা চেয়েছেন? অথবা ফেইথ হিলিংকে বুজরুকি বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন?”
‘Psychic’ (অতীন্দ্রিয়) কোনও কিছুই ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। ফেইথ হিলিং-এর বিষয়ে আমাকে কয়েক জায়গায় এই ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে। যাঁরাই এই ধরনের প্রশ্ন করেছেন বলেছি, দুঃখিত, ব্যাখ্যা আমার জানা নেই। তাদের অনুরোধ করেছি ব্যাখ্যা চেয়ে আমার মেডিটেশন ও কনসেনট্রেশনে বিঘ্ন সৃষ্টি করবেন না।
“আরও একটা কথা কী জানেন মিস্টার ঘোষ, বিজ্ঞান এগিয়েছে বলে ঈশ্বর মিথ্যে হয়ে যায়নি। পৃথিবীর বহু দেশের টেলিভিশন কোম্পানি ফেইথ হিলিং-এর উপর ছবি তুলেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ অনেক উল্টোপাল্টা অভিযোগও তুলেছে। ওদের অভিযোগ, অস্ত্রোপচারের সময় যে রক্ত ও দেহাংশ ওরা সংগ্রহ করেছিল সেগুলো পরীক্ষা করিয়ে নাকি দেখছে ওসব মানুষের দেহাংশ ওরা সংগ্রহ করেছিল সেগুলো পরীক্ষা করিয়ে নাকি দেখছে ওসব মানুষের দেহাংশ বা রক্ত নয়। কিন্তু পৃথিবীর কোনও যুক্তিবাদী মানুষের কাছেই অভিযোগগুলো গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেনি। কারণ পরীক্ষার আগে সংগৃহীত নমুনা পাল্টে দেওয়ার সবরকম সুযোগই পরীক্ষকদের ছিল। এই সুযোগ যে তাঁরা গ্রহণ করেননি, তার গ্যারাণ্টি কে দেবে?”
“একটু সহজ করে বোঝাবার চেষ্টা করছি। আপনার ওপর অস্ত্রোপচার করলাম। আপনি সেই অস্ত্রোপচারের ছবি তুলে রাখলেন। আমাকে দিয়ে আজই যে অস্ত্রোপচার করিয়েছেন, তার সপক্ষে আরও কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করে রাখলেন। ধরুন, আপনি ফেইথ হিলিং-এ বিশ্বাস করেন না। যেহেতু আপনি বিশ্বাস করেন না, তাই আপনি চান অন্যেরাও যাতে আমার হিলিংকে অবিশ্বাস করে, আমাকে প্রতারক ভাবে। আমাকে প্রতারক প্রমাণ করতে আপনি এক টুকরো তুলোয় মাছের রক্ত মাখিয়ে কোনও হাসপাতাল বা ল্যাব-এ পরীক্ষা করতে দিলেন। তারা পরীক্ষা করে লিখিতভাবে জানিয়ে দিলেন তুলোয় সংগৃহীত রক্ত মাছের। আপনি এর পর যদি কোনও নামী-দামী পত্রিকায় ঢাউস প্রবন্ধ লিখে আমাকে প্রতারক আখ্যা দেন এবং প্রমাণ হিসেবে আপনার শরীরে আমি অস্ত্রোপচার করছি এমন ছবি ছাপেন, রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট ছাপেন, তাতে কিছু যুক্তিহীন মানুষ হয় তো বিভ্রান্ত হতে পারেন, কিন্তু কোনও যুক্তিবাদী মানুষই আপনার কথাকে চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে মেনে নেবেন না। কারণ এক্ষেত্রে নমুনা পাল্টানোর সুযোগ আপনার ছিল, এবং আপনার সততার বিষয়টি একেবারেই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে দাঁড়িয়ে থাকে।
“প্রতিটি যুক্তিবাদী মানুষ আপনার প্রমাণকে চূড়ান্ত বলে মেনে নিতেন, আপনার কথায় আস্থা রাখতেন, যদি রক্তের নমুনা পুলিশ দপ্তর থেকে সংগৃহীত ও সরকারি ফরেনসিক দপ্তর থেকে পরীক্ষিত হত। সে সব টিভি কোম্পানি বা ওই জাতীয় প্রতিষ্ঠান আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন, আসলে তাঁরাই মিথ্যাচারী, সস্তায় বাজিমাত করতে চেয়েছেন। তাই সংগৃহীত নমুনা পাল্টে দেওয়ার সুযোগও নিজেদের হাতে রেখেছিলেন।
“আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তিবাদী বলে বিজ্ঞাপিত জাদুকর জেমস র্যাণ্ডি তাঁর লেখা একটা বইতে এক উদ্ভট তথ্য সরবরাহ করেছেন। বলেছেন—ফেইথ হিলাররা নাকি নিজেদের বুড়ো আঙুলে একটা নকল বুড়ো আঙুলের খাপ পরে থাকে। ওই খাপের মধ্যে লুকানো থাকে রক্ত। তারপর তিনি আমাদের ঠগ, জালিয়াত ইত্যাদি বলে চেঁচিয়েছেন। আপনি আমার দু’হাত দেখুন। কোথাও বুড়ো আঙুলের খাপ দেখতে পাচ্ছেন?” হাত দুটো এগিয়ে দিলেন মিস্টার গ্যালার্ডো।
“এই মুহূর্তে আপনি শুয়ে পড়ুন, আপনার শরীর থেকে এখনই ডেভিল ব্লাড বার করে দিচ্ছি, দেখতে পারেন কোনও কৌশল নেই।” বললেন মিস্টার গ্যালার্ডো।
আমি আশ্বস্ত করলাম, ‘আপনাকে অবিশ্বাস করার মতো কোনও কিছুই ঘটেনি। কিন্তু একটা প্রশ্ন, আপনারা সাংবাদিকদের এড়াতে চাইছেন কেন? এতে কেইথ হিলিং-এর সত্যতা সম্বন্ধে সংবাদপত্রগুলোর সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক নয় কি?”
“এই বিষয়ে বলতে পারবেন মিস্টার আগরওয়াল।”
আগরওয়ালকে প্রশ্নটা করতে বললেন, “যাঁরা সন্দেহ করতে চান করুন, তাঁদের মিথ্যে সন্দেহে আমাদের কিছুই আসে যায় না।”
“আমাকে কেন তবে সাক্ষাৎকার নেওয়ার অনুমতি দিলেন?”

“আপনার কথা স্বতন্ত্র। আপনার ফেইথ হিলিং-এ বিশ্বাস আছে, নিজেরও চিকিৎসা করাবেন, তমোনাশের রেফারেন্সের লোক, তাই আপনার অনুরোধ ঠেলতে পারিনি। সত্যি বলতে কী, আপনি যদি খবরের কাগজে আমাদের সম্বন্ধে এক লাইনও না লেখেন তো খুবই উপকার হয়। খবর পড়ে যখন ভিড় বাড়বে তখন ভিড় সামলায় কে? সবারই উপকার করতে ইচ্ছে তো হয়, কিন্তু আমাদের খাটার ক্ষমতারও এক সীমা আছে।” বললেন মিস্টার আগরওয়াল।
“পেশেণ্টদের মধ্যে বাঙালি কেমন আসছেন?”
আগরওয়াল বললেন, “খুব কম। দিনে দু-একজন। কিছু মনে করবেন না, হাজার টাকা খরচ করার মতো বাঙালি খুব কমই আছেন।” মিস্টার গ্যালার্ডোকে এবার জিজ্ঞেস করলাম, “আপনার বয়েস কত?”
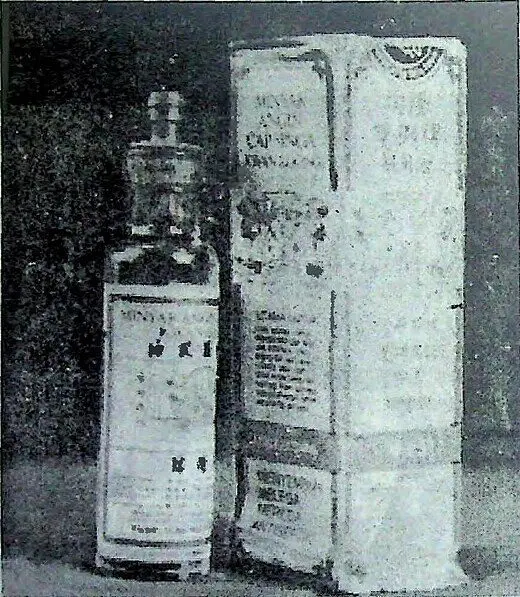
“আমি তেতাল্লিশ, মিসেস উনচল্লিশ।”
“ফিলিপিন্স-এ কতজন ফেইথ হিলার আছেন?”
“প্রথম শ্রেণির ফেইথ হিলারের সংখ্যা আমাকে নিয়ে দশ জন। এছাড়াও দ্বিতীয় শ্রেণির জনা চল্লিশ ফেইথ হিলার আছেন।”
বললাম, “শুনেছি প্রথম শ্রেণির ফেইথ হিলারদের রাজনৈতিক ক্ষমতা অত্যধিক?”
“সব দেশের স্পিরিচুয়ালিস্টরাই এই ক্ষমতা পেয়ে থাকেন। আপনাদের দেশেও তার বাইরে নয়।” বললেন, মিস্টার গ্যালার্ডো।
আমাদের কথাবার্তার মাঝে ছবি তুলে যাচ্ছিল জ্ঞান ও সৌগত। মিস্টার গ্যালার্ডো বললেন, “লেখাটা প্রকাশিত হওয়ার পর একটা কপি মিস্টার আগরওয়ালকে দয়া করে পাঠিয়ে দেবেন, তাহলেই আমি পেয়ে যাব।”
“নিশ্চয়ই দেব।”
“এবার আপনার, শারীরিক সমস্যাটা বলুন।”

বললাম, “সমস্যা তিনটি। গলায় ফ্যারেনজাইটিস, হার্টেও কিছু অসুবিধে রয়েছে, একটা স্ট্রোক হয়েছিল, গলব্লাডারের আশেপাশে মাঝে-মধ্যে খুব ব্যথা হয়।”
গ্যালার্ডোর আহ্বানে অপারেশন টেবিলে খালি গায়ে শুয়ে পড়লাম। এখন আমার টেবিলের এক পাশে দেওয়ালের দিকে পিঠ করে মিস্টার গ্যালার্ডো। মাথার দিকে এক গাদা তুলো হাতে মিসেস গ্যালার্ডো। মিস্টার গ্যালার্ডোর বাঁ পাশে একটা টুলের উপর রয়েছে এক বালতি জল আর একটা বড় সাদা তোয়ালে। ডানপাশে আর একটা খালি বালতি। আমার সামনে ছোট-খাট একটা ভিড়। এঁদের অনেকেই রোগী এবং তাঁদের আত্মীয়-স্বজন। আমাদের সমিতির এক নজরদার সভ্যকেও দেখতে পেলাম।

মিস্টার গ্যালার্ডো আমার পাশে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে হাত দুটো কিছুটা মেলে দিয়ে চোখ বুজে বিড়বিড় করে কী যেন বললেন। তারপর কিছুটা জল ও একটা রামজাতীয় স্বচ্ছ তরল ওষুধ নিয়ে আমার পেটে, বুকে ও গলায় আধ-মিনিটের মতো মালিশ করলেন। হাত দুটো এবার জলের বালতিতে ডুবিয়ে আমার গলার বাঁ পাশে গ্যালার্ডো তাঁর দু-হাতের আঙুল চেপে ধরে হঠাৎ আঙুলগুলো কচ্লাতে লাগলেন। চট্ করে একরকম আওয়াজ হচ্ছিল। অনুভব করলাম আমার গলা বেয়ে তরল কিছু নেমে যাচ্ছে। বুঝলাম রক্ত। মিস্টার গ্যালার্ডো তাঁর ডান হাতটা আমার চোখের সামনে ধরলেন। কালচে লাল থকথকে কিছু। হাতের থকথকে ময়লা ডান পাশের বালতিতে ফেলে হাতটা জ্বলের বালতিতে ডুবিয়ে ধুয়ে নিলেন। পাশের তোয়ালেতে হাতটা মুছে নিলেন। ইতিমধ্যে গড়িয়ে পড়া রক্তধারার কিছুটা মিসেস গ্যালার্ডো পরম মমতায় তাঁর হাতের তুলো দিয়ে মুছে দিলেন।
এরপর একে একে খালি হাতে আমার গলব্লাডার ও হার্টে অস্ত্রোপচার করলেন গ্যালার্ডো। অস্ত্রোপচার শেষে একটা ঘটনা ঘটল। মিসেস গ্যালার্ডো তুলো হাতে এগিয়ে এলেন রক্ত মুছিয়ে দিতে। এটাই সঠিক মুহূর্তে। শোয়া অবস্থাতেই আমি ওঁর হাতের তুলো থেকে কিছুটা ছিঁড়ে নিয়ে পেট থেকে গড়িয়ে পড়া রক্ত নিলাম। দ্রুত এগিয়ে এলেন সুবিমল দাশগুপ্ত। আমার হাত থেকে তুলোটা নিয়ে একটা টেস্ট টিউবে ঢুকিয়ে মুখ বন্ধ করে টেস্ট টিউবটা পকেটে পুরলেন। সকলের দৃষ্টি যখন পুরোপুরি এই ঘটনার দিকে তখন সাধ্যমতো তৎপরতার সঙ্গে প্যাণ্টের ডান পকেট থেকে রুমালটা বের করে পেট থেকে গড়িয়ে পড়া রক্তের কিছুটা মুছে নিয়ে রুমালটা আবার পকেটেই চালান করে দিলাম।
কিছুটা থতমত গ্যালার্ডো আমার গলায়, বুকে ও পেটের সামান্য উপরে জল ও বাম-জাতীয় স্বচ্ছ তেল আধ মিনিটের মতো মালিশ করে ছেড়ে দিলেন।
উঠে বসে শার্ট গায়ে গলাতেই মিস্টার গ্যালার্ডো বললেন, “এখন কেমন লাগছে?”
“ভালো, অনেকটা ভালো। এখন আমার শরীর ঘিরে বাম ঘষার মতো একটা ঝাঁজালো ঝিরঝিরে ভাব।”
“কাল আর পরশু আর দুদিন আসুন। বার-তিনেক হিলিং করালে আশা করি অনেক তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবেন।” বললেন, মিস্টার গ্যালার্ডো।
আমি ঘড়ি দেখলাম। আমার উপর মোট তিনটে অস্ত্রোপচারে সময় লেগেছে পাঁচ মিনিট।
আমি ওঠার পর সুবিমলবাবু শুলেন। ওঁর কপালে ব্যথা। আরও দ্রুততর গতিতে হাত চালাতে লাগলেন বিশ্বখ্যাত ফিলিপিনো ফেইথ হিলার রোমেও পি. গ্যালার্ডো। এরপর আমরা আরও চারজন রোগীর উপর অস্ত্রোপচার দেখলাম ও ছবি তুললাম। কয়েকজন রোগী ও তাঁদের আত্মীয়দের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বুঝলাম অলোক খৈতান সত্যিই এমন রহস্যময় চিকিৎসার যোগ্য ব্যবস্থাপক। প্রত্যেককেই ইতিমধ্যে নিখুঁত টিমওয়ার্ক মারফত মুখ খুলতে বারণ করে দিয়েছেন। একজন মাত্র মহিলার কাছ থেকে বহু কষ্টে তাঁর ঠিকানা জোগাড় করতে সক্ষম হয়েছিলাম। সেই ঠিকানাও সেদিন জোগাড় করেছিলাম লিটন হোটেল থেকে বেশ কিছুটা দূরে, হোটেলের চার দেওয়ালের ভিতর তিনিও কোনও অজ্ঞাত কারণে আমাদের যথেষ্ট ভীতির চোখে দেখছিলেন। মহিলাটি তাঁর নাম বলেছিলেন অঞ্জলি সেন। রোগী তাঁরই ছেলে। দেখে মনেহল খুবই রুগ্ণ এবং কিছুটা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন।
আমরা বিদায় নেওয়ার আগে অলোক আমাকে বললেন, “কাজটা ঠিক করলেন না। মিস্টার গ্যালার্ডো আপনাদের বলতে বলেছিলেন, শয়তানের রক্ত পকেটে নিয়ে ঘোরা ঠিক নয়, এতে অপঘাতে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। ডেভিল ব্লাড মিস্টার গ্যালার্ডোর হাতে তুলে দিলেই বোধহয় ভালো করবেন।”
বুঝলাম প্রচ্ছন্ন হুমকি। হেসে ‘গুডবাই’ জানিয়ে বিদায় নিলাম আমরা। পরের দিন ৭ তারিখ রবিবার বিকাল চারটের সময় আবার হোটেল লিটনে গেলাম। এই সময় সুবিমলবাবুরও থাকার কথা। গিয়ে তাঁর দেখাও পেলাম। হোটেলের উপর নজর রাখা সমিতির কিছু সভ্যর কাছ থেকে পাওয়া কয়েকটা খবরের ভিত্তিতে বুঝেছিলাম জল অনেক দূর গড়িয়েছে। যে খবরগুলো জানানো প্রয়োজনীয় মনে হল সুবিমলবাবুকে সেগুলি দিলাম। গ্যালার্ডো আমার ও সুবিমলবাবুর উপর হিলিং করলেন। আজ গ্যালার্ডো, অলোক এবং আগরওয়াল আমাকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একই প্রশ্ন করলেন, ‘ফেইথ হিলিং সম্পর্কে আপনার মতামত কী?’
বললাম, “সত্যিই বিস্ময়কর।”
তৃতীয় দিন, সোমবার ৮ সেপ্টেম্বর, সকাল থেকে পরপর কয়েকটা ঘটনা ঘটে গেল।
সকাল ৭টা ৫০। এক তরুণ আমার ফ্ল্যাটে এলেন বিশাল এক মোটর বাইক আরোহী। এঁকে আমি হোটেল লিটনের কনফারেন্স রুমে দেখেছি। বসতে বলে জিজ্ঞেস করলাম, “আপনি কোথা থেকে আসছেন ভাই?”
নিজের কোনও পরিচয় বা আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তরুণটি সরাসরি আমাকেই প্রশ্ন করলেন, “ব্লাড টেস্টে কী পেলেন খুবই জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।”
“এই কথা জিজ্ঞেস করতে আমার কাছে এসেছেন? আপনার তৎপরতার প্রশংসা না করে পারছি না। এত তাড়াতাড়ি আমার বাড়িতে আপনাদের আশা করিনি। ব্লাড স্যাম্পেল যাঁর কাছে, প্রশ্নটা সেই সুবিমল দাশগুপ্তকেই করা উচিত ছিল আপনার।”
অফিসে যেতেই আমার ঘরে দেখা করতে এলো জ্ঞান। জানাল, আজ অফিস আসতে গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউয়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফুটপাত ছেড়ে রাস্তায় নামতেই একটা মোটর পিছন থেকে এসে ওকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। এ ধরনের ভাবার কারণ, মোটরটাকে দেখেই জ্ঞানের মনে পড়েছে সকাল থেকে বার কয়েক বাড়ির ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখার সময় এই গাড়িটাকে উল্টো ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল এবং গাড়িটা রং সাইডে ড্রাইভ করে জ্ঞানের ঠিক পিছনে নিয়ে আসা হয়। গাড়ি কোনও হর্ন দেয়নি। গাড়ির শব্দ শুনে পিছনে তাকিয়ে ফুটপাতে লাফিয়ে পড়ে জ্ঞান। গাড়িটাও দ্রুত পালিয়ে যায়। নম্বর দেখার কোনও সুযোগ পায়নি।
সকালে আমার বাড়ির ঘটনা এবং জ্ঞান মল্লিকের ঘটনা ফোনে লালবাজারে সুবিমল দাশগুপ্তকে জানালাম। সুবিমলবাবু আমাকে বললেন আজ যেন কোনও রকমভাবে ফেইথ হিলিং না করাই। দুপুরের মধ্যে হোটেলে নজর রাখার দায়িত্ব থাকা সমিতির দুই সভ্য খবর দিলেন, আজ একটা বড় রকমের অঘটন ঘটতে পারে, আমি যেন সাবধান হই।
বিকেল ঠিক পাঁচটার সময় হোটেলের বাইরে জ্ঞান আর সৌগত রায়বর্মনকে পেলাম। দুজন আমাকে দেখে স্বস্তি পেল। ওদের কাছে খবর পেলাম দুজনকেই নাকি আজ বিভিন্ন জায়গায় অনুসরণ করা হয়েছে। আমরা তিনজনে হোটেলের কনফারেন্স রুমে ঢুকলাম। ভিতরে যথেষ্ট ভিড়। আমাকে দেখে এগিয়ে গেলেন এলেন মিস্টার অলোক খৈতান। বললেন, “আজ একটু দেরি হচ্ছে। আপনি আজও হিলিং করাবেন তো?”
বললাম, “সেই জন্যেই তো আসা।”
অলোক বললেন, “একটু অপেক্ষা করতে হবে। মিস্টার গ্যালার্ডোর আজ মেডিটেশন ঠিক মতো হচ্ছে না বলেই এই দেরি।”
ভিড়ের মধ্যে আমাদের সমিতির দুজন সভ্যকেও দেখতে পেলাম। আমরা তিনজন হোটেলের বাইরে এলাম। ঠিক করলাম ওয়াই এম সি এ-তে বসে কথা বলব। এখানেও আমাদের পিছনে টিকটিকি। ঝুলবারান্দায় বসে ওমলেট আর চা খেতে খেতে আমরা ঠিক করলাম আজ আর হিলিং করাব না, কারণ আজ হোটেলে যেন বড় বেশি সন্দেহজনক চরিত্রের আনাগোনা। শুধু বিদায় নিয়ে আসব ওদের কাছ থেকে। হোটেলে ঢোকার মুখেই অলোকের সঙ্গে দেখা, আমাকে দেখে এগিয়ে এসে বললেন, “দাদা, আজ দুপুরে সেণ্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরের সঙ্গে আপনি দেখা করেছেন খবর পেলাম। ডিরেক্টর সাহবের ব্লাড রিপোর্ট কী বলছে?”
“আমার শরীর থেকে আমারই রক্ত বের হবে। সুতরাং তার রিপোর্ট কী, এ নিয়ে আপনাদের কেন এত মাথা ঘামাবার প্রয়োজন হলো বুঝতে পারছি না। দেখা করেছি সে খবর জানতে পারলেন, আর তিনি কী বলছেন, সে খবর জানতে পারলেন না?”
আমার কাছ থেকে এই ধরনের কিছু উত্তরই বোধহয় প্রত্যাশা করেছিলেন। আমার কথা শোনার পরেও বিনয়ী হাসি হেসে বললেন, “আজ মিস্টার গ্যালার্ডো কারও হিলিং করবেন না। আপনি বরং কাল আসুন।”
একটি পত্রিকা অফিস থেকে সন্ধে ছ’টা নাগাদ যোগাযোগ করলাম সুবিমলবাবুর সঙ্গে। পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে তাকে ওয়াকিবহাল করে রাখলাম। সব শুনে সুবিমলবাবু বললেন, “ফরেনসিক রিপোর্ট পেতে একটু দেরি হবে। তোমার রুমালের দাগ দেখে ব্লাড ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর সত্যেনবাবু কী বললেন?”
“বললেন, দাগ দেখে আমার মনে হচ্ছে এটা কোনও মানুষের রক্তের নয়। এই ধরনের রুমালের সামান্য দাগ পরীক্ষা করে বলার মতো আধুনিক যন্ত্রপাতি আমাদের নেই! একমাত্র ফরেনসিক টেস্টই আসল সত্য নিখুঁতভাবে উদ্ঘাটনে সক্ষম।”
ফেইথ হিলার গ্যালার্ডো জলের সঙ্গে যে তেল মিশিয়ে রোগীর শরীরে মালিশ করে, তারই একটা শিশি রাত এগারোটায় আমার বাড়িতে এসে পৌঁছে দিয়ে গেলেন খৈতান শিবিরেরই এক ব্যক্তি। বিনিময়ে তাঁর একটি উপকার অবশ্য আমাকে করতে হয়েছিল।
চতুর্থ দিন, ৯ তারিখ, মঙ্গলবার দুপুরের পর খবর এল গ্যালার্ডো দম্পতি লিটন হোটেল ছেড়ে, এয়ারপোর্ট হোটেলে উঠছেন।
সন্ধ্যায় একটি পত্রিকার অফিস থেকে ফোনে যোগাযোগ করলাম সুবিমলবাবুর সঙ্গে। ইতিমধ্যে আমার কাছে খবর এসেছে, আজই গ্যালার্ডো দম্পতি ভারত ত্যাগ করছেন। সুবিমলবাবু সেই সঙ্গে জানালেন, “প্রদীপ সরকারকে (জাদুকর) আজই ফেইথ হিলার আর তোমার কথা জানালাম। ওর ধারণা ফেইথ হিলার সম্ভবত নিজের আঙুলে ছুঁচ বা ওই ধরনের কোনও কিছু ফুটিয়ে রক্ত বের করে রোগীর শরীরে মাখিয়ে দিচ্ছে।”
বললাম, “আপনি তো বেশ কয়েকটা অপারেশন দেখলেন। আর প্রতিটি অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রেই বেরিয়ে আসা রক্তের পরিমাণ যথেষ্ট। একটা রোগীর ক্ষেত্রে যদিও এইভাবে রক্ত দেখানো সম্ভব বলেও ধরে নিই, কিন্তু বহুজনের ক্ষেত্রে পদ্ধতি সম্পূর্ণ অসম্ভব।”
আমার যুক্তিটা সুবিমলবাবুর মনে ধরেছে মনে হল। বললেন, “তা বটে। কিন্তু রহস্যটা তুমি ধরতে পেরেছ?”
“নিশ্চয়ই। আগামী রবিবার সকালে আমার বাড়িতে চলে আসুন। ছেলের উপর একইভাবে অস্ত্রোপচার করে দেখাব।”
রবিবার ১৪ সেপ্টেম্বর সুবিমলবাবু না এলেও ভারতীয় যুক্তিবাদী সমিতির সভ্যদের সামনে ছেলে পিনাকীর উপর একইভাবে অস্ত্রোপচার করে দেখালাম। পিনাকীর পেট ফুটো হয়ে আমার ডান হাতের আঙুলগুলো ঢুকে গেল। বেরিয়ে এল রক্ত। তারপর শরীরের ভিতর থেকে বের করে আনলাম এক টুকরো মাংস। ছবি তুললেন চিত্র-সাংবাদিক গোপাল দেবনাথ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সমিতির সদস্য, কয়েকজন সাংবাদিক ও চিত্র-সাংবাদিক। সকলেই যদিও জানতেন আমি কৌশলের সাহায্যে অস্ত্রোপচার করছি, তবুও উপস্থিত কেউই আমার কৌশলটা কোথায়, সেটা বুঝতে না পেরে যথেষ্ট অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।
সব শেষে উপস্থিত দর্শকদের সামনে প্রকাশ করলাম কৌশলটা। অস্ত্রোপচারের পূর্ব মুহূর্তে আমার পোশাকের আড়াল থেকে খালি হাতে এসে গিয়েছিল একটা পাতলা রবারের ছোট্ট বেলুন। বেগুনি রঙের ওই বেলুনে পোরা ছিল নকল রক্ত। আমার হাতের ভিতর বেলুনটা এমন কৌশলে লুকিয়ে রেখেছিলাম যে দর্শকরা মুহূর্তের জন্যেও আমার হাতে বেলুনের অস্তিত্বের কথা বুঝতে পারেননি। পিনাকীর পেটে হাতের আঙুলগুলোকে এমন কৌশলে স্থাপন করেছি, সাধারণের দৃষ্টিতে মনে হয়েছে ওর পেট ফুটো করেই বুঝি আমার আঙুলগুলো ঢুকে গেল। বেলুনটাকে চট্কে ফাটাতেই নকল রক্ত ছড়িয়ে পড়েছে। বেলুনের ছেঁড়া কালচে-লাল রবারকেই থকথকে দেহাংশ বলে দেখিয়েছে। আর পিনাকীর পেট থেকে যে মাংসের টুকরোটা ছিঁড়ে এনেছিলাম আসলে সেটা ছিল তুলোর ভাঁজে লুকানো। গ্যালার্ডো অবশ্যই আমারই কায়দায় প্রতিবারই অস্ত্রোপচারের আগে কখনও পোশাকের আড়াল থেকে কখনও বা পাশের তোয়ালের ভাঁজ থেকে নকল রক্ত ঠাসা বেলুন তুলে নিয়েছেন এবং জাদুর পরিভাষায় যাকে বলে ‘পামিং’ সেই ‘পামিং’ করেই বেলুন লুকিয়ে রেখেছেন দর্শকদের এবং ক্যামেরার চোখ এড়িয়ে তারপর যা করেছেন তার বর্ণনা তো আমার করা অস্ত্রোপচারের পদ্ধতিতেই দিয়েছি।
পোশাকের আড়ালে বিশেষ কৌশলে অনেক জাদুকর অনেক কিছুই লুকিয়ে রাখেন। একে ম্যাজিকের পরিভাষায় বলে ‘লোড নেওয়া’। পোশাকের আড়ালে এ-ভাবেই জাদুকরেরা লুকিয়ে রাখেন পায়রা, খরগোশ, এমনি আরও কত না জিনিস-পত্তর।
ঘটনাটা এখানেই শেষ করা যেত, কিন্তু এরপর আরও দু-একটা ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না। প্রথম ঘটনাটি ঘটল ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ রবিবার দুপুর ২-১৫ মিনিটে। অলোক খৈতান বাড়িতে এলেন। জানতে চাইলেন, ফেইথ হিলিং বিষয়ে আমার অভিমত কী।
বললাম, পুরো ব্যাপারটাই ধাপ্পা। পিনাকীর ওপর আমার খালি হাতে অস্ত্রোপচারের (ফেইথ হিলিং-এর) ছবিও দেখালাম অলোককে। ধাপ্পাটা কেমনভাবে দেওয়া হয় সেটাও বোঝালাম!
সব শোনার পর অলোক আমাকে জানালেন, এবার আমি গোলমাল পাকিয়ে দেওয়ায় পুরোপুরি পরিকল্পনা মাফিক চলতে না পারায় এঁদের অনেক আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। আমি সহযোগিতা করলে অলোক খৈতান ও রামচন্দ্র আগরওয়াল পরবর্তী পর্যায়ে ম্যানিলা থেকে দু-জন ফেইথ হিলার নিয়ে আসবেন এবং কলকাতায় এক মাস ধরে দু-জনকে দিয়ে ফেইথ হিলিং করাবেন। আমি সহযোগিতা করলে প্রতিদিন তিনজন রোগীর দেওয়া ফিস আমি পাব। অর্থাৎ প্রতিদিন ১৫ হাজার টাকা। এক মাসে ৪,৫০,০০০ টাকা। এছাড়া আমাকে ম্যানিলার নিয়েও যাবেন যখন অলোক বা রামচন্দ্র ম্যানিলায় ফেইথ হিলারের সঙ্গে চুক্তি করতে যাবেন। আলোচনা চালিয়ে গেলাম—প্রস্তাবটা আর কত দূর পর্যন্ত ওঠে জানতে। শেষ পর্যন্ত অলোক আমাকে প্রতিদিন দশ জন রোগীর দেওয়া টাকা দেবেন বলে সর্বোচ্চ প্রস্তাব দিলেন, অর্থাৎ প্রতিদিন ৫০,০০০ টাকা। তিরিশ দিনে ১৫,০০,০০০ টাকা আমার কথায়-বার্তায় অলোক যথেষ্ট উৎসাহিত হয়েই অনেক খোলামেলা কথা বললেন, তিনি জানতেন না, তাঁর ও আমার কথাগুলো টেপ রেকর্ডারে টেপ হয়ে যাচ্ছে।
২৯ তারিখ অলোক আমার অফিসে ফোন করেন আমার মতামত জানতে। তাঁকে জানাই, “পৃথিবীতে চিরকালই কিছু বোকা লোক থাকেন বাঁরা অর্থের কাছে নিজেদের বিক্রি করেন না। আমিও এই ধরনেরই একজন বোকা লোক বলেই ধরে নিন। আমি পত্রিকায় আপনাদের ফেইথ হিলিং নিয়ে লিখছি। আমাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করবেন না। গতকাল আপনার সঙ্গে আমার যা কথা হয়েছিল তা সবই টেপ করেছি। ইতিমধ্যে ক্যাসেটের কয়েকটা কপি কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির হাতে চলে গেছে। আমার কোনও বিপদ হলে তাঁরা ক্যাসেটগুলো হাজির করবেন। টাকার জোরে এদের সকলকেই আপনি কিনে নেবেন ভেবে থাকলে ভুল করবেন, কারণ এঁদের পরিচয় আপনি কোনও দিনই পাবেন না, আমি ছাড়া আর কেউই জানেন না কার কাছে ক্যাসেটের কপি আছে।”
অলোক আমার উপর একটা চ্যালেঞ্জেই ছুড়ে দিলেন। বললেন, “আপনি কোন্ পত্রিকায় ছাপবেন? দেখুন আপনার লেখা ছাপানো আমি বন্ধ করতে পারি কি না।”
এর কয়েক দিন পরেই সৌগতের তোলা ফেইথ হিলিং-এর কিছু নেগেটিভ ‘পরিবর্তন’ পত্রিকা অফিসের নেগেটিভ লাইব্রেরি থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গেল!
১৪ নভেম্বর মহাজাতি সদনের দোতলায় ‘বর্তমান ফিলিপাইন’ বিষয়ক এক আলোচনা চক্রে এবং ২৪ নভেম্বর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ফোরাম অফ সায়েণ্টিফিক ভ্যালুজ’ আয়োজিত এক অলৌকিক-বিরোধী আলোচনা চক্রে ফিলিপিনো ফেইথ হিলারের রহস্য নেগেটিভ-এর রহস্যময় অন্তর্ধান বিষয়ে শ্রোতাদের অবগত করি। ১৫ লক্ষ টাকার বিনিময়ে অলোক খৈতানের সহযোগিতা প্রার্থনার ঘটনা উপস্থিত শ্রোতাদের জানিয়ে এই সংগ্রামে প্রয়োজনে আমার ও আমাদের সমিতির পাশে তাঁদের দাঁড়াতে আহ্বান জানাই। ২৪ ডিসেম্বর ’৮৬, বুধবার আমার শরীরে অস্ত্রোপচারের সময় সংগ্রহ করা রক্তের ফরেনসিক রিপোর্ট দেখতে পেলাম। তাতে পরিষ্কার বলা আছে, রক্তের নমুনাটি পশুর। রিপোর্টটার কিছুটা অংশ তলায় দিলাম—
Result of Examination
Ruminant animals blood was detected in the stains on ‘A’ (cotton) (Vide the enclosed original report No. 9053 / MLR dt. 16.12.86. of the Serologist Govt. of India).
Sd/-S. K. Basu 22.12.86.
ফেইথ হিলার ও জাদুকর পি. সি. সরকার (জুনিয়র)
১৯৮৭-র ২০ আগস্ট আজকাল পত্রিকায় ‘চিটিং ফাঁক’ সিরিজে ‘ছুরি-কাঁচি ছাড়া অপারেশন’ শিরোনামে জাদুকর পি সি সরকার (জুনিয়র)-এর একটি লেখা প্রকাশিত হয়। লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণের মধ্যে তীব্র বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। শ্রীসরকার ‘ফেইথ হিলার’কে ‘স্পেশাল ডাক্তার’ নামে অবহিত করে তাঁর প্রতিবেদনে জানান, রোগীর শরীরে অস্ত্রোপচারের সময় স্পেশাল ডাক্তার তার নিজের আঙুলের ফাঁকে একটা আলপিন ঢুকিয়ে নিজের শরীর থেকে রক্ত বের করে। সাধারণ দর্শক স্পেশাল ডাক্তারের শরীর থেকে বের হওয়া রক্তকেই রোগীর শরীর থেকে অস্ত্রোপচারের জন্য বেরিয়ে আসা রক্ত বলে ভুল করেন। কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ তাই রোগীর দেহে লেগে থাকা রক্তের নমুনা ফরেনসিক পরীক্ষা করে স্পেশাল ডাক্তারের অস্ত্রোপচার ধাপ্পা কি না ধরতে গিয়ে ঠকে গেছেন। কারণ ফরেনসিক রিপোর্টে দেখা গেছে রক্তটা মানুষেরই।
শ্রীসরকারের এই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হওয়ার এক মাস আগে ২০ জুলাই ’৮৭-তে আনন্দবাজার পত্রিকায় ‘কলকাতার কড়চা’ কলমে লৌকিক—‘অলৌকিক’ শিরোনামে একটি খবর প্রকাশিত হয়, তাতে জানানো হয়েছিল:
অজ্ঞান না করে, স্রেফ খালি হাতে, ব্যথাহীন অস্ত্রোপচারে রোগ সারানোর কৌশল জানা আছে বলে দাবি করেন ‘ফেইথ হিলার’রা। সেই ফেইথ হিলার’দের নিয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে চলছে রীতিমতো হৈচে। সম্প্রতি ম্যানিলা থেকে গৌহাটি হয়ে কলকাতায় এসে রোমিও পি গ্যালার্ডো আর তার স্ত্রী রোজিও গ্যালার্ডো অলৌকিক চিকিৎসক হিসেবে আসর জমিয়ে বসেছিলেন। এঁরা দুজনে মিলে নাকি দিনে দুশজন পর্যন্ত রোগীর রোগমুক্তি ঘটাচ্ছিলেন। একেকজনের অস্ত্রোপচারে সময় লাগছিল মাত্র তিন থেকে পাঁচ মিনিট। আর ফি মাত্র পাঁচ হাজার টাকা। অস্ত্রোপচার শেষে রোগীর দেহে সামান্যতম দাগও নাকি খুঁজে পাচ্ছিলেন না কেউ। বেশ চলছিল এসব অবিশ্বাস্য কাজকর্ম। এমন সময়ে আসরে এলেন ‘র্যাশনালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়া’র সম্পাদক প্রবীর ঘোষ। নিজের আসল পরিচয় লুকিয়ে তিনি উঠলেন গ্যালার্ডোর অপারেশন টেবিলে। অপারেশনের পুরো দৃশ্যটা ভিডিও ক্যামেরায় ধরে রাখলেন তাঁর দুই সঙ্গী। আর অস্ত্রোপচারের পর প্রবীরবাবু নিজের শরীরে লেগে থাকা রক্ত তুলোয় মুছে, তা তুলে দিলেন দুদে পুলিশ অফিসার সুবিমল দাশগুপ্তের জিম্মায়। রক্তাক্ত তুলো ‘সীল’ করা হল ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য। ব্যাপার-স্যাপার দেখে গ্যালার্ডো দম্পতি তড়িঘড়ি কলকাতা থেকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে পালালেন ম্যানিলায়। ইতিমধ্যে ফরেনসিক রিপোর্টে মিলেছে এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। রক্তের নমু মানুষের নয়। পশুর। যুক্তিবাদী প্রবীরবাবু বিভিন্ন সমাবেশে দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন অলৌকিক বলে প্রচারিত লোক ঠকানো ‘ফেইথ হিলিং’ বা ‘সাইকিক সার্জারি’-র লৌকিক কৌশল। আর এক কাজে প্রবীর ঘোষকে চিঠিপত্রে প্রায়শই উৎসাহ জোগাচ্ছেন অলৌকিক-বিরোধী জনপ্রিয় মার্কিন লেখক জেমস র্যাণ্ডি।
বিভ্রান্তির কারণ তিনটি। প্রথমত প্রতিদিন একশো থেকে দুশোজন রোগীর শরীরে অস্ত্রোপচার করার ক্ষেত্রে নিজের শরীরের রক্তকে রোগীর শরীরের রক্ত বলে বিশ্বাস স্থাপন করাতে কম করেও যে পরিমাণ রক্ত নিজের শরীর থেকে বের করা প্রয়োজন সেই পরিমাণ রক্ত বের করার পরও স্পেশাল ডাক্তারের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব কি না? বিশেষত স্পেশাল ডাক্তার যেহেতু প্রতিদিনই এই সংখ্যক রোগীদের শরীরে অস্ত্রোপচার করে চলেছেন।
দ্বিতীয়ত, আঙুলের ফাঁকের অংশে শরীরের ভিতর আলপিন ফুটিয়ে অত বিপুল রক্ত বের করা আদৌ বাস্তবসম্মত চিন্তার ফসল নয়, বিশ্বাসযোগ্য নয়।
তৃতীয়ত, কলকাতার গোয়েন্দা দপ্তর যে রক্তের নমুনা অস্ত্রোপচারকালীন সংগ্রহ করেছিল তার ফরেনসিক রিপোর্ট বিষয়ে শ্রীসরকার বলেছেন—রক্তের নমুনা ছিল মানুষেরই। আমার বক্তব্য হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে—ফরেনসিক রিপোর্ট ছিল রক্তের নমুনা পশুর। আমাদের দুজনের পরস্পরবিরোধী কথায় উভয় পত্রিকার পাঠকরা বিভ্রান্ত হয়েছেন। ফরেনসিক রিপোর্ট বিষয়ে আমাদের দুজনের মধ্যে একজন কেউ নিশ্চয়ই ভুল বা মিথ্যে তথ্য পরিবেশন করেছি।
জানতাম, আমার উপর মিথ্যা সন্দেহের বোঝা বিচ্ছিন্নভাবে শুধু আমার ক্ষেত্রে নয়, আমাদের সমিতির সততা বিষয়টিও আসতে বাধ্য, যা যুক্তিবাদী আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, ব্যাহত করবে। এক্ষেত্রে আমার পক্ষে নীরবতা পালন বিভ্রান্তিই বাড়াবে মাত্র। তাই বিজ্ঞান আন্দোলনে স্বার্থে, যুক্তিবাদী আন্দোলনের স্বার্থেই শ্রীসরকারের প্রসঙ্গকে টেনে আনতে বাধ্য হলাম।
বিভ্রান্ত পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে বেশ কিছু চিঠি এই প্রসঙ্গে পেয়েছি। তাঁদের প্রত্যেকেরই মূল বক্তব্য ছিল—আমাদের দুজনের মধ্যে কে সত্য কথা বলছি। আমার বক্তব্য যদি সত্যিই হয়, তবে মুখ খুলছি না কেন? বহু চিঠির ভিতর থেকে এখানে দেবদর্শন চক্রবর্তী, তথাগত চট্টোপাধ্যায় ও আদৃতা মুখোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরিত চিঠিটির উল্লেখ করছি। চিঠিতে তাঁরা জানিয়েছেন:
আমরা যৌথভাবে আনন্দবাজার পত্রিকার ‘সম্পাদক সমীপেষু’ বিভাগে এবং আজকাল পত্রিকার ‘প্রিয় সম্পাদক’ বিভাগে দুটি চিঠি পাঠিয়েছি। চিঠি দুটির প্রতিলিপি আপনার কাছে পাঠালাম। এই বিষয়ে আপনার মতামত আমরা প্রকাশ্যে জানতে আগ্রহী, আপনি নীরব থাকলে আমরা অবশ্যই ধরে নেব, আপনি মিথ্যা প্রচারের সুযোগ নিয়ে যশ, প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে ইচ্ছুক একজন ধূর্ত ভণ্ড ও প্রতারক। এই একই চিঠি আমরা জাদুকর পি সি সরকার (জুনিয়র)-কেও পাঠিয়েছি। আশা রাখি, আমাদের এই সত্যকে জানার যুক্তিনিষ্ঠ প্রচেষ্টাকে আপনারা দুজনেই স্বাগত জানিয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন।
যে দুটি চিঠি তাঁরা পাঠিয়েছিলেন, তার প্রতিলিপি এখানে তুলে দিচ্ছি—
৩১ আগস্ট ১৯৮৭
‘প্রিয় সম্পাদক’
আজকাল
৯৬, রাজা রামমোহন সরণি
কলকাতা-৭০০০৯
জাদুকর পি সি সরকার (জুনিয়র) ‘চিটিং ফাঁক’-এর নামে যে সব তথ্য ও তত্ত্ব পরিবেশন করছেন; সেগুলোর বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ থেকে যাচ্ছে। জাদুকর সরকারকে বিনীত অনুরোধ, জাদু নিয়ে থাকুন, জাদু নিয়ে লিখুন, কিন্তু রাতারাতি বিজ্ঞানমনস্ক সাজতে যাবেন না। বিজ্ঞানমনস্ক সাজা যায় না, হতে হয়।
জাদুকর সরকার একজন অলৌকিকত্বের ধারক-বাহক। তাঁর কথায়—আমার মতে আত্মা জিনিসটা সম্পূর্ণ বাস্তব, কিন্তু চলতি বিজ্ঞান এখনও তাকে ঠিক মতো সমঝে উঠতে পারেনি। তিনি আর এক জায়গায় বলেছেন, ‘ভূত সম্পর্কে আমরা জানি না বুঝি না বলে উড়িয়ে দেওয়া মোটেই ঠিক নয়। বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা কেউই কিন্তু উড়িয়ে দেননি।’ আরও সুন্দর কথাও তাঁর কলমে আমরা পড়েছি—‘আজকে যেটাকে ভৌতিক ভাবছি, আগামী দিনে সেটা হয়ত পরিষ্কার বিজ্ঞান বলে পরিচিত হবে।’
এই তিনটি উক্তি তোলা হয়েছে, ‘কিশোর মন’ পত্রিকায় ‘অমর আত্মার কাহিনি’ রচনা থেকে।
জাদুকর সরকারের এইসব বিজ্ঞান-বিরোধী কথার এখানে শেষ নয়। তিনি নিজেও নাকি এক ভূতের কাছ থেকে উপকার পেয়েছেন।
জাদুকর সরকার ঈশ্বরের অস্তিত্বেও বিশ্বাসী; অলৌকিকত্বে
বিশ্বাসী। তারও বহু উদাহরণ ছড়িয়ে আছে তাঁরই
বহু লেখায়। তাঁর মতো এমন একজন বিজ্ঞান-
বিরোধী শিবিরের মানুষকে কুসংস্কারের
বিরুদ্ধে বিজ্ঞানমনস্কদের পক্ষে প্রচার
চালাতে দেখলে শঙ্কিত হই।
শঙ্কা আরও বাড়ে যখন দেখি ভেজাল ধরতে গিয়ে তিনি নিজেই ভেজাল দিচ্ছেন।
২০ আগস্টের লেখায় যাঁদের তিনি ‘স্পেশাল ডাক্তার’ বলেছেন, তাঁদের প্রকৃত টার্মটা তাঁর জানা ছিল না বলেই কি তাদের ওই নামে অবহিত করেছেন? এনসাইক্লোপিডিয়ায় চোখ বুলোলে তিনি ‘ফেইথ হিলার’দের কথা নিশ্চয়ই পেতেন। তিনি কি জানেন পৃথিবীর বহু দেশ ফেইথ-হিলারদের নিয়ে তথ্যচিত্রও তুলেছে? ফেইথ হিলাররা ঠিক সেই ধরনের চিটিংবাজ নয়, অতিসরলীকরণ করে যে ভাবে জাদুকর সরকার তাঁদের চিত্রিত করেছেন।
জাদুকর সরকারের মতে, নিজের আঙুলে আলপিন ফুটিয়ে স্পেশাল ডাক্তার অপারেশনের রক্ত বার করেন। এই পদ্ধতিতে কোনোরকমভাবেই এক নাগাড়ে মাত্র পাঁচজন রোগীর উপরও অস্ত্রোপচার চালানো সম্ভব নয়; অথচ ফেইথ হিলাররা দিনে একশোর উপরও অপারেশন করে থাকেন। শ্রীসরকারকে বিনীত অনুরোধ, কোনো বিষয় না জেনে সে সম্পর্কে অন্যকে জানানোর বাসনা সংযত করুন।
জাদুকর পি সি সরকারের যে বক্তব্যের সার অনুসন্ধানের জন্য মূলত আমাদের এই চিঠি লেখা, তা হল, শ্রীসরকার তাঁর লেখাটিতে জানিয়েছেন কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ রোগীর দেহে লেগে থাকা রক্তের নমুনার করেনসিক পরীক্ষা করে দেখেছেন, এটি মানুষের রক্ত।
২০ জুলাই আনন্দবাজার পত্রিকায় ‘কলকাতার কড়চা’য ‘লৌকিক-অলৌকিক’ নামে একটি ফিচার প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল, র্যাশনালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়ার সম্পাদক প্রবীর ঘোষ নিজের পরিচয় গোপন করে, খালি হাতে ব্যথাহীন অস্ত্রোপচারের জন ফেইথ হিলার গ্যালার্ডোর অপারেশন টেবিলে ওঠেন। অস্ত্রোপচারের পর প্রবীরবাবুর শরীর থেকে বেরিয়ে আসা রক্ত সংগ্রহ করেন পুলিশ অফিসার সুবিমল দাশগুপ্ত। ফরেনসিক পরীক্ষায় দেখা যায় রক্তের নমুনা পশুর। ব্যাপার দেখে গ্রেপ্তার এড়াতে গ্যালার্ডো দম্পতি কারবার গুটিয়ে পালিয়েছেন ম্যানিলায়।
ফেইথ হিলারদের ফরেনসিক রিপোর্ট নিয়ে যুক্তিবাদী প্রবীর ঘোষ ও জাদুকর পি সি সরকার (জুনিয়র)-এর মধ্যে যে কেউ একজন ভুল বা মিথ্যে খবর পরিবেশন করেছেন। যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে শ্রীঘোষের বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিগুলি জাদুকর সরকারের অতীন্দ্রিয় বিষয়গুলির ব্যাখ্যার চেয়ে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হয়। যুক্তিবাদী মানুষ হিসেবে আমরা প্রকৃত সত্যের মুখোমুখি হতে চাই। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলে সহযোগিতা করলে বাধিত হব।
স্বাক্ষর : দেবদর্শন চক্রবর্তী
(রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ)
স্বাক্ষর : তথাগত চট্টোপাধ্যায়
(অর্থনীতি বিভাগ)
স্বাক্ষর : আদৃতা মুখোপাধ্যায়
(ইংরাজী বিভাগ)
প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা।
৩১ আগস্ট ১৯৮৭
সম্পাদক সমীপেষু
আনন্দবাজার পত্রিকা
৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০১
২০ শে জুলাই আনন্দবাজার পত্রিকায় ‘কলকাতার’ কড়চা’য় ‘লৌকিক-অলৌকিক’ নামে একটি ফিচার প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল, র্যাশনালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়ার সম্পাদক প্রবীর ঘোষ নিজের পরিচয় গোপন করে খালি হাতে ব্যথাহীন অস্ত্রোপচারের জন্য ফেইথ হিলার গ্যালার্ডোর অপারেশন টেবিলে ওঠেন। অস্ত্রোপচারের পর প্রবীর ঘোষের শরীর থেকে বেরিয়ে আসা রক্ত সংগ্রহ করে ফরেনসিক পরীক্ষায় পাঠান পুলিশ অফিসার সুবিমল দাশগুপ্ত। ফরেনসিক পরীক্ষায় দেখা যায় রক্তের নমুনা মানুষের নয়, পশুর।
২০ আগস্ট ‘আজকাল’ পত্রিকার ‘চিটিং-ফাঁক’ কলমে ফেইথ হিলারের উপরে ‘ছুরি কাঁচি ছাড়া অপারেশন’ শীর্ষক একটি লেখা প্রকাশিত হয়। লেখক জাদুকর পি সি সরকার (জুনিয়র)। শ্রীসরকার জানিয়েছেন, কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ রোগীর দেহে লেগে থাকা রক্তের নমুনার ফরেনসিক পরীক্ষা করে দেখেছেন, এটি মানুষের রক্ত।
দুই পত্রিকার দুই বিপরীত বক্তব্যে আমরা বিভ্রান্ত। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পত্রিকা দুটি এবং শ্রী ঘোষ ও শ্রী সরকারের সহযোগিতা কামনা করি।
প্রেসিডেন্সি কলেজের পক্ষে
আদৃতা মুখোপাধ্যায় (ইংরাজি বিভাগ)
তথাগত চট্টোপাধ্যায় (অর্থনীতি বিভাগ)
দেবদর্শন চক্রবর্তী (রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ)
আবারও বলি, এই জাতীয় বক্তব্যের প্রচুর চিঠি আমি পেয়েছি। এর উত্তরে অতি স্পষ্ট করে বক্তব্য রাখার একান্ত প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে জানাচ্ছি:
১। কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তর কলকাতায় আসা ফিলিপিনো ফেইথ হিলার বা ‘স্পেশাল ডাক্তার’-এর অস্ত্রোপচার করার সময় একবারই মাত্র রক্ত সংগ্রহ করেছিলেন।
২। রক্ত সংগ্রহ করেছিলেন সেই সময়কার কলকাতা পুলিশের যুগ্ম-কমিশনার সুবিমল দাশগুপ্ত।
গু। আমার শরীরে অস্ত্রোপচারকালে বেরিয়ে আসা রক্তই সুবিমল দাশগুপ্ত সংগ্রহ করেছিলেন।
৪। রক্তের নমুনার ফরেনসিক পরীক্ষার ফল আগেই তুলে দিয়েছি। তাতে স্পষ্টতই জানানো হয়েছে রক্তের নমুনা ছিল পশুর।
৫। পি সি সরকার (জুনিয়র)-এর ‘আজকাল’ পত্রিকায় প্রকাশিত ফেইথ হিলার সম্পর্কিত লেখাটির বিষয়ে সুবিমল দাশগুপ্ত অবহিত হয়েছিলেন। এবং শ্রীসরকারের বক্তব্যে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং একই সঙ্গে আন্তরিকভাবে দুঃখিত হয়েছিলেন।
প্রসঙ্গত জানাই, ফিলিপিন বেতার ও দূরদর্শন থেকে ফেইথ হিলার প্রসঙ্গে আমাকে নিয়ে একটি অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় ১৯৯০ সালে।
পরলোক থেকে আসা বিদেহী ডাক্তার
‘পরিবর্তন’ সাপ্তাহিক পত্রিকায় ১৯৮৪ সালের ১৮ জানুয়ারি সংখ্যায় যে প্রচ্ছদ কাহিনি প্রকাশিত হয়ে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছিল সেটির শিরোনাম হল—পরলোক থেকে আসা বিদেহী ডাক্তার মৃত্যুপথযাত্রী রোগীকেও বাঁচিয়ে তুলছেন। লেখক— আনন্দস্বরূপ ভাটনাগর। মূল প্রতিবেদনটি সাপ্তাহি ‘হিন্দুস্থান’-এ প্রকাশিত হয়েছিল। সেখান থেকে অনুবাদ করে লেখাটি প্রকাশ করে ‘পরিবর্তন’। অনুবাদক রুমা শর্মা।
প্রতিবেদনটি শুরু হয়েছিল এইভাবে:
যিনি রোগাক্রান্ত হন, তিনি সাধারণত চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের কাছে যান। কেউ পছন্দ করেন অ্যালোপ্যাথি। কেউ হোমিওপ্যাথি কেউবা কবিরাজি। ইদানীং শোনা যাচ্ছে আকুপাংচার করে রোগ উপশমের কথা।
কিন্তু পরলোক থেকে ডাক্তার এসে রোগ নিরাময় করছেন এ খবর নতুন। বিদেশেও হ্যারি এডওয়ার্ড একই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করে হাজার হাজার মৃত্যুপথযাত্রী রোগীকে বাঁচিয়েছেন।
কী তাদের চিকিৎসা পদ্ধতি? রোগী রোগিণীদেরই বা প্রতিক্রিয়া কী? তারই বিস্তৃত প্রতিবেদন।
প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছিল:
‘পরলোক সম্বন্ধে ধারণা’
বাস্তবে যে ব্যক্তি ইহলোকে সারা জীবন ডাক্তারী করে গেছেন পরলোকে গিয়েও তাঁর যে ইচ্ছা থেকে যায়। আমাদের চিন্তাই আমাদের ব্যক্তিত্বের আধার এবং ঠিক সেভাবেই আমরা নিজস্ব কার্যকলাপ অনুধাবন করি। সে চিন্তাচ্ছন্নতাই মৃত্যুর পরও আমাদের সঙ্গে থেকে যায়। অধিকাংশ লোকের পরলোক সম্বন্ধে ভুল ধারণা রয়েছে। তাঁরা ভাবেন সূক্ষ্মলোকে হয়তো ভূত-প্রেত রয়েছে বা মৃত্যুর পর আত্মা খুব তাড়াতাড়ি অন্যত্র দেহধারণ করে। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। সূক্ষ্মলোকতত্ত্ব এবং তাতে জীবনের গতিবিধি একটি স্বতন্ত্র বিষয়। মূলত একথা বলা যেতে পারে যে এ জগতের শ্রেষ্ঠ এবং পবিত্র আত্মাগণ যাঁরা সঙ্গীতজ্ঞ, নাট্যকার, যোগী, কলাকার প্রভৃতি আপন সাধনায় নিমগ্ন থাকেন তাঁদেরই ভেতর থাকেন সে সব পরোপকারী আত্মা, যাঁরা ভূ-পৃথিবীতে নেমে এসে নানারকম ভাবে মানুষকে সাহায্য করেন। পরলোকপ্রাপ্ত ডাক্তাররাও রোগীর সেবায় রত থাকতে চান। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁরা কোন সুপাত্রের মাধ্যমে লোক সেবা করেন। যাঁরা উদার হৃদয় ও ধার্মিক স্বভাবসম্পন্ন তাঁদেরই মাধ্যমে তাঁরা রোগীর অসাধ্য রোগ উপশম করেন।
১৯৩৫-এর কথা। হ্যারি এডওয়ার্ডকে তাঁর এক বন্ধু একটি চার্চে নিয়ে যান। সেখানে এক আত্মার মাধ্যমে তাঁকে বলা হয় যে, তাঁর মধ্যে রোগ উপশম করার প্রতিভা রয়েছে। একই ভাবে অন্য চার্চেও সেই মাধ্যম দ্বারা তাঁকে একই কথা বলা হয়। তাই তিনি ভাবলেন, একটু চেষ্টা করে দেখাই যাক না। সে সময় তাঁরই এক বান্ধবীর বন্ধু ইংলণ্ডের ক্রম্পটন হাসপাতালে মরণাপন্ন অবস্থায় শয্যাশায়ী ছিলেন। তিনি ক্ষয় রোগাক্রান্ত ছিলেন। হৃদপিণ্ডের স্ফীতি হওয়াতে ভেতরের নাড়ি ফেটে রক্তস্রাব হচ্ছিল। সেখানেই হ্যারি এডওয়ার্ড তাঁর সম্পূর্ণ নীরোগ হওয়ার কামনা করে মন একাগ্র করলেন। এক সপ্তাহ পর যখন তিনি তাঁর বান্ধবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, তিনি বললেন, তাঁর বন্ধুর হৃদপিণ্ডের স্ফীতি এখন আর নেই। রক্তস্রাবও বন্ধ হয়ে গেছে। একথা শুনে তিনি অত্যন্ত উৎসাহিত বোধ করলেন এবং সেইভাবেই রোগীর রোগ উপশম করার চেষ্টায় ব্রতী হলেন। কিছুদিন পর সেই রোগী সুস্থ হয়ে পুনরায় নিজের কাজে যোগ দেন।
eএকদিন হ্যারি এডওয়ার্ড নিজের ছাপাই ও স্টেশনারি দোকানে অন্যান্য দিনের মতো কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এমন সময় এক মহিলা দোকানের ভেতরে এসে বললেন, কে যেন তাঁকে এই দোকানে ঢোকার জন্য প্রেরণা দিচ্ছে। তাই তিনি এসেছেন। তিনি বললেন, তাঁর স্বামী লণ্ডনে একটি হাসপাতালে বক্ষ ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে অনেকদিন শয্যাশায়ী ছিলেন। হাসপাতালের ডাক্তারেরা তাঁর নীরোগ হওয়ার সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। যে কটা দিন তিনি বেঁচে আছেন, সে কটা দিন তিনি বাড়িতে ফিরে গিয়ে যেন হাসিখুশিতে বাকি জীবনটা কাটান—এ উপদেশ দিয়েছেন।
বিদেহী আত্মার দ্বারা প্রতিকার
সেই মহিলার মনোকষ্টে হ্যারি এডওয়ার্ড অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং তাকে আশ্বাস দিলেন যে তাঁর স্বামীর চিকিৎসা তিনি বিদেহী ডাক্তারের মাধ্যমে করবেন। কিন্তু এ কথা বলা যত সহজ ছিল, বক্ষ ক্যানসার আক্রান্ত রোগীর রোগ উপশম করা ততই সন্দেহজনক মনে হতে লাগল। রাতে তিনি মন একাগ্র করে সেই বিদেহী আত্মার কাছে তাঁর নীরোগ হওয়ার প্রার্থনা করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই সে রোগী খুব তাড়াতাড়ি সুস্থতা লাভ করে কাজে মনোনিবেশ করলেন। কিছুদিন পর মহিলাটি তাঁর স্বামীকে নিয়ে গেলেন হাসপাতালে পরীক্ষা করবার জন্য এবং তিনি ডাক্তারদের জানালেন, যে দিন থেকে তিনি হাসপাতাল ছেড়ে বাড়ি ফিরেছেন সেদিন থেকেই কোনো প্রকার পথ্য গ্রহণ করেননি। ডাক্তাররা অবিশ্বাসের হাসি হেসে বললেন, তাঁদের নির্ধারিত ওষুধের গুণেই তিনি সুস্থতা লাভ করেছেন।
এইভাবে হ্যারি এডওয়ার্ড তার জীবনের প্রথম দুটি ক্ষেত্রে অত্যন্ত অচিন্ত্যনীয়ভাবে সফলতা পেয়ে গেলেন তাঁর স্পিরিচুয়াল হিলিং-এর মাধ্যমে। একে অ্যাবসেণ্ট হিলিং বলা হয়। অতঃপর তিনি নিজের সম্পর্কে নিশ্চিত্ত হলেন যে তাঁর ভেতর রোগ উপশম করার ক্ষমতা রয়েছে। একদিন একটি মেয়ে মধ্যরাত্রে তাঁর ঘরে এসে জানালেন যে তাঁর বোন জ্বরাক্রান্ত হয়ে বেঘোরে পড়ে আছে এবং তার সঙ্গে অন্যান্য কিছু উপসর্গও দেখা দিয়েছে। ডাক্তারেরা জবাব দিয়েছেন। তিনি এক পরাশক্তি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সিদ্ধ ব্যক্তির আদেশে হ্যারি এডওয়ার্ডের কাছে এসেছেন। সে রাত্রেই তাঁকে অ্যাবসেণ্ট হিলিং দেওয়া হল। দ্বিতীয় দিন সকালে হ্যারি এডওয়ার্ড তাঁদের বাড়িতে গিয়ে বোনটির মাথায় হাত রেখে মঙ্গল কামনা করলেন। সে দিনটা বৃহস্পতিবার ছিল। হ্যারি এডওয়ার্ড জানালেন যে মেয়েটি সপ্তাহখানেক পরেই সুস্থ হয়ে উঠবেন। পরিবার পরিজনেরা তাঁর দিকে অবিশ্বাস্যভাবে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু দেখা গেল রবিবার সকালে সে মেয়েটি বিছানায় বসে চা পান করছে এবং তার জ্বরও একদম ছেড়ে গেছে। অতঃপর দেখা গেল যে, সে মেয়েটি ক্ষয় রোগাক্রান্ত এবং পনেরো দিন অন্তর তাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হত এবং বায়ু সেবন করা হত। হ্যারি তাঁর এই নবার্জিত প্রয়াসকে অক্ষুণ্ণ রেখে কাজ করে চললেন। ক্ষয় রোগ থেকে মুক্তি পেল মেয়েটি। হাসপাতালের ডাক্তারেরা তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ বলে ঘোষণা করলেন। পরবর্তীকালে মেয়েটি সেই হাসপাতালে নার্সের কাজ পেয়েছে এবং এখন সেই কাজেই আছে। এভাবে শরীর স্পর্শ করে চিকিৎসার পদ্ধতিটিতে এই প্রথমবার তিনি সফলতা লাভ করলেন। এটি কনটাক্ট হিলিং-এর দৃষ্টান্ত।
অতঃপর হ্যারি এডওয়ার্ডের বাড়িতে রোগীরা ভিড় করে আসতে লাগলেন। স্পিরিচুয়াল হিলিং-এর মাধ্যমে তাঁরা নিরাময় লাভ করে রীতিমতো উপকৃত হলেন। এখানে এই মহান মানুষ ও অপার্থিব চিকিৎসাটি সম্পর্কে কিছু বলা যেতে পারে।
২৯ মে, ১৮৯৩ সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ৪২ বৎসর বয়সে তিনি বিদেহী আত্মার মাধ্যমে রোগ উপশম চর্চা শুরু করেন। এবং ১৯৭৬-এর ৯ ডিসেম্বর তাঁর পার্থিব দেহ পরলোকে লীন হয়। মরদেহ ত্যাগ করে সূক্ষ্মলোকে গমন করেন তিনি, সেখানে বিদেহী ডাক্তারদের মধ্যে স্থিত হন অতঃপর। ৪১ বৎসর পর্যন্ত পৃথিবীর অনেক অসাধ্য রোগীর রোগ উপশম করে তাদের রোগ মুক্ত করেছেন এই প্রয়াত মানুষটি। তাঁর বিদেহী আত্মার আরোগ্য-মন্দিরে প্রত্যেক সপ্তাহে কয়েক হাজার চিঠি আসত এবং প্রত্যেকটি চিঠির তিনি উত্তর দিতেন। ১৯৫৫ সন পর্যন্ত তিনি দশ লক্ষ চিঠির জবাব দেন। তাঁর স্বর্গপ্রাপ্তির পর আজও হ্যারি এডওয়ার্ড সেনচুরির কাজকর্ম সে প্রকারই করা হয়।
অসাধ্য রোগের চিকিৎসা
ভারতবর্ষে এখনও অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁরা হ্যারি এডওয়ার্ডের অ্যাবসেণ্ট হিলিং-এর মাধ্যমে রোগ উপশম করে আরোগ্যলাভ করেছেন। ১৯৭০-এর আগস্ট মাসে ২৭ বৎসর বয়স্কা কুমারী ছায়ার পায়ে স্ফোটক হয়। কয়েক বৎসর বিভিন্ন পদ্ধতিতে তার চিকিৎসা করানো হয় কিন্তু কিছুতেই তাকে সারানো যাচ্ছিল না। অতঃপর সে হ্যারি এডওয়ার্ডের কাছে তিন মাস ধরে চিঠিপত্র লেখালেখি করতে লাগল এবং আশ্চর্যের ব্যাপার সব কটি চিঠির উত্তরও পেল। একদিন সকালে সে উঠে দেখে কোন দৈববলে যেন তার স্ফোটক একেবারে উধাও হয়ে গেছে।
হ্যারি এডওয়ার্ড ইংলণ্ডের একটি জাঁকজমকপূর্ণ আলো ঝলমলে বিশাল সভাকক্ষে হাজার হাজার দর্শকের সামনে বিদেহীরূপে এসে তাঁর অত্যাশ্চর্য চিকিৎসা পদ্ধতিতে আরোগ্যলাভ হওয়ার প্রক্রিয়া প্রদর্শন করতেন। রয়েল অ্যালবার্ট হলে একবার তাঁর এরকম একটি ঘটনার সময় দিল্লির স্পিরিচুয়াল হিলার শ্রীমতী স্বর্ণনারঙ্গ উপস্থিত ছিলেন। এই প্রদর্শন কক্ষে জনৈক জটিল রোগাক্রান্ত রোগীকে একটি মঞ্চের ওপর এসে দাঁড়াতে বলা হল। এক যুবক তার অতি বৃদ্ধা মাকে কোলে করে নিয়ে এসে সেই মঞ্চের ওপর দাঁড় করাল কোনক্রমে। সেই বৃদ্ধার সম্পূর্ণ শরীর যাতে আক্রান্ত ছিল। মাইকে এসে তিনি অস্ফুট শব্দে বললেন, “বাছা তুই আমার শরীরের আর কী ভালো করবি! কিন্তু এতটুকু উপকার কর যাতে আমার আঙুলগুলো অদ্ভুত সোজা হয়ে যায়, আমি যেন নিজের হাত দিয়ে নিজের খাবারটুকু খেতে পারি। আমার ছেলে, নাতির হাত দিয়ে তুলে দেওয়া খাবার মুখে নিতে বড় লজ্জা করে।” দর্শকরা হেসে উঠলেন হো হো করে। এর কিছুক্ষণ পরেই সেই বৃদ্ধা নিজের চেষ্টায় আস্তে আস্তে মঞ্চের উপর সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। খুব খানিকটা হাত-পা ছোড়াছুড়ি করতে শুরু করলেন, আবার একটু দৌড়েও নিলেন আনন্দে এভাবে হ্যারি এডওয়ার্ড তাঁর রোগ নিরাময় ক্ষমতা দেখিয়ে দিলেন পৃথিবীর মানুষের চোখের সামনে।
বিদেহী ডাক্তার দ্বারা আরোগ্যলাভ
বোম্বের হাসপাতালে বহু বিদেশি ডিগ্রিধারী এক প্রতিভাবান ডাক্তার রয়েছেন, রমাকান্ত কোনি। তিনি বৃদ্ধ-অবস্থার যে কোন ধরনের রোগ নিবারণে বিশেষজ্ঞ। প্রথম জীবনে অ্যালোপ্যাথি পদ্ধতিতেই চিকিৎসা শুরু করেছেন। ডা. রমাকান্ত কোনি সারস্বত ব্রাহ্মণ হলেও বিবাহ করেছেন অস্ত্রের প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী রস্তাকে, যিনি ছিলেন গৌড়-ব্রাহ্মণ।
১৯৭২ সনে ডা. কোনি কোমরের স্পনডিলোসিস-এ আক্রান্ত হয়ে অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। মেরুদণ্ডের অসহ্য ব্যথার দরুন তিনি শয্যাগত হন। ভাবলেন, বাকি জীবনটা বোধহয় বিছানায় শুয়েই কাটাতে হবে। সে সময় তাঁর জনৈক বয়স্ক বন্ধু তাঁকে হ্যারি এডওয়ার্ডের কাছে আরোগ্য কামনা করে চিঠি লেখার জন্য উৎসাহিত করলেন। আধুনিক মনোভাবাপন্ন এবং সুশিক্ষিত হওয়ার দরুন তিনি এ বিষয়টি প্রথমে বিন্দুমাত্র বিশ্বাসযোগ্য মনে করতে পারেননি। কিন্তু বন্ধুর কথা রাখবার জন্য তিনি তাঁকে চিঠি লিখলেন। নিজের এবং অন্যান্য ডাক্তারদের এ বিষয় আশ্চর্য ভাবান্তর দেখা দিল এবং তিনি খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠলেন।
বিচিত্র ঘটনা
১৯৭২ সনে একটি বিচিত্র ঘটনা ঘটে। এতে ডাক্তার রমাকান্ত কোনির জীবনে নতুন এক অধ্যায় শুরু হয়। এ অবস্থায় তাঁর একটি ‘সিয়ানস’ দেখার সুযোগ হল। ঘর অল্প অন্ধকার ছিল। লোকেরা চেয়ারে গোল হয়ে বসেছিলেন। মধ্যস্থলে যে মিডিয়াম, সে ঘুরে ঘুরে এক একটি লোকের কাছে এসে তাঁদের মৃত আত্মীয়স্বজনদের সম্বন্ধে সংবাদ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এক সময় ঘুরে এসে ডা. কোনির সামনে দাঁড়ালেন। এবং বললেন ‘আমার বিদেহী মাৰ্গদর্শক জানাচ্ছেন যে আপনাকে রোগ উপশম করার প্রতিনিধি (যন্ত্র) সাব্যস্ত করা হয়েছে, যাতে আপনার মাধ্যমে বিদেহী ডাক্তার দ্বারা রোগীর রোগ উপশম করা যায়।’ বারবার তাঁকে এ কথা বলা হল। তিনি বললেন ‘আপনি নিজের মন হাতে সমস্ত সন্দেহ, শঙ্কা ও দ্বন্দ্ব দূর করে ফেলুন।’
এই বৈঠকের পর আমার মনে এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হল। মনে হল কেউ যেন আমার অন্তরে অফুরন্ত শক্তি জুগিয়ে দিয়েছে। আমি যেন মাইলের পর মাইল দৌড়ে চলে যেতে পারি। আমার পিঠে যেন দুটো ডানা লাগানো হয়েছে। আমার মনের এই বিচিত্র আত্মবিশ্বাস ও আনন্দ উপলব্ধি করে আমি প্রায় উম্মাদ হয়ে উঠলাম। আমার হাতের ছোঁয়া মাত্র রোগী নীরোগ হয়ে উঠবে বলে মনে হতে লাগল। করতল উষ্ণ হয়ে উঠল। আঙুলের প্রান্তগুলোতে যেন তরঙ্গ বয়ে যেতে লাগল। চোখ বুজতেই জ্যোতির্ময় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডতে স্ফুলিঙ্গের ছটা দেখা দিতে লাগল। এই বিচিত্র অনুভূতির কথা তিনি তাঁর নিজের লেখা বই ‘সাইকো হিলিং’-এ বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি বোম্বের একজন সুবিখ্যাত মিডিয়ামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁর সহযোগিতায় নিজের বিদেহী মার্গদর্শক সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করলেন। সূক্ষ্মলোক নিবাসী তিনি দুশো বৎসর আগে এ লোকে থাকাকালীন অবস্থায় সার্জারি ও ডাক্তারি করে গেছেন এবং এখনও তিনি পরলোকে অবস্থান করে নানা প্রকার অনুসন্ধান করে চলেছেন। তিনি এরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন যশস্বী ডাক্তার ছিলেন যে জটিল রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ করা মাত্র বুঝতে পারতেন রোগী কোন রোগে আক্রান্ত হয়েছে। ডাক্তার কোনিকে মাধ্যম হিসেবে উপযোগী করে তাঁর ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করে তিনি রোগ উপশম করেন। ডা. কোনি যখন রোগীর শরীর স্পর্শ করেন তাঁর আঙুলগুলো রোগীর রোগাক্রান্ত স্থানটির প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে এবং তিনি খুব তাড়াতাড়ি রোগ নির্ণয় করে ফেলেন। ওষুধ লেখার সময়ও তিনি অনুভব করেন যেন কেউ তাঁর হাত ধরে ওষুধগুলোর নাম লিখিয়ে নিচ্ছেন যেমন ‘অটোমেটিক রাইটিং’-এ লেখা হয়। অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ও অ্যালোপ্যাথি ডিগ্রি বিভূষিত এই আধুনিক ডাক্তার ভদ্রলোক না জানি কত দুরূহ রোগীর রোগ নিরাময় করে তাদের সুস্থ সবল করেছেন। অনেক কঠিন রোগ নিরাময় করার সম্বন্ধে বর্ণনা তাঁর কাইলে লিপিবদ্ধ রয়েছে। মাত্র অ্যাবসেণ্ট হিলিং দ্বারাই তিনি ১৯৮১ সন পর্যন্ত ২৭০০ রোগীর রোগ উপশম করেছেন। ভারতে শুধু বোম্বের হাসপাতালেই এই স্পিরিচুয়াল হিলিং-এর ব্যবস্থা রয়েছে।
কনট্যাক্ট হিলিং
যে সব রোগী নানা পদ্ধতিতে নিজেদের চিকিৎসা করিয়ে শ্রান্ত ও নিরাশ হয়ে পড়েন তাঁরাই অবশেষে ডা. কোনির কাছে আসেন বিদেহী চিকিৎসার জন্য। বিশ্বাসের অভাব তো রয়েছেই তাঁদের মনে, তবু তাঁরা শঙ্কিত হৃদয়ে এই চিকিৎসা পদ্ধতিটিকেও যাচাই করে নিতে চান। অন্যান্য চিকিৎসা ক্ষেত্রে তাঁরা ধৈর্য সহকারে সুস্থ হওয়ার আশা রাখেন। তবে বিদেহী আত্মার দ্বারা চিকিৎসা করাতে এসে মনে করেন যেন তাঁদের অসুস্থতা জাদুমন্ত্রে উড়ে যাবে এবং সম্পূর্ণ নীরোগ হয়ে খুব তাড়াতাড়ি হাসপাতাল হতে বেরিয়ে আসবেন। কিন্তু এ ব্যবস্থায় যে কোনো রোগ যতদিনকারই হোক সারার কথা, তাতে ধৈর্য হারালে চলে না ৷
প্রতিবেদন প্রসঙ্গে কিছু কথা
প্রতিবেদনটির শুরুতে প্রতিবেদক মৃত্যুর পর আত্মা বাস্তবিকই কী করে—বলতে গিয়ে যা বলেছেন তা একান্তভাবেই প্রতিবেদকের নিজস্ব বিশ্বাসের কথা। তাঁর এই বিশ্বাসের পিছনে কোনও পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ কাজ করেনি। যুক্তি বা বিজ্ঞান সিদ্ধান্তে পৌঁছায় পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণের পথ ধরে। বিশ্বাস চলে আপন খেয়াল-খুশিতে। কখনও বহু লোকে বিশ্বাস করে, বিখ্যাত ব্যক্তিরা বিশ্বাস করেন, এই কু-যুক্তিতে মানুষ অন্ধভাবে কোনও কিছুতেই বিশ্বাস স্থাপন করেন। কখনও শাস্ত্রবাক্য, গুরুবাক্য ইত্যাদিকে অভ্রান্ত বলে ধরে নেওয়া থেকে সৃষ্টি হয় অন্ধ বিশ্বাস। বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তির লড়াই জন্মলগ্ন থেকেই। কারও একাত্ত ব্যক্তি বিশ্বাস কখনই বিজ্ঞানের সত্য হয়ে উঠতে পারে না, তা সেই বিশ্বাস আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ বা সত্যজিৎ রায় যাঁরই হোক না কেন। যুক্তির সত্য, বিজ্ঞানের সত্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই আসবে পরীক্ষা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই।
এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। কলিকাতা পুস্তকমেলা ’৯০-এ আমাদের সমিতিও আসর জাঁকিয়ে বসেছিল এক রঙিন ছাতার তলায়। প্রতিদিনই আমরা নানা অনুষ্ঠান ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে পৌঁছতে চেষ্টা করছিলাম। এক সন্ধায় এক বিশপ আমাদের সামনে কিছু প্রশ্ন তুলেছিলেন। এই ধরনের প্রশ্ন আরও বহু ভাববাদীদের কাছ থেকে আসার সম্ভাবনা আছে বলেই প্রসঙ্গটির অবতারণা করছি।
বিশপ আমাকে বলেছিলেন, “কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশ্বাস রাখতেই হয়, এমনই একটি ক্ষেত্র ঈশ্বর। ঈশ্বরকে বিশ্বাসেই পাওয়া যায়, যুক্তিতে নয়। যুক্তিতে সব কিছু প্রমাণ করা যায় না। আপনার বাবারই যে আপনি ছেলে তা কি আপনি প্রমাণ করতে পারেন? পারেন না। এখানে আপনাকে বিশ্বাসের উপরই নির্ভর করতে হয়।”
বলেছিলাম, গর্ভধারণ যিনি করেছেন তিনিই আমার যা। এবং তাঁর স্বামীকেই আইনত আমি ও সমাজ বাবা বলে স্বীকার করে নিয়েছে। নিশ্চয়ই যুক্তির দিক থেকে যে কোনও সন্তানেরই জন্ম হতে পারে সাধারণভাবে সক্ষম নারী-পুরুষের মিলনে। সেই মিলন বিবাহিত স্বামীর সঙ্গে না হতেও পারে। এই সম্ভাবনা আপনার আমার সবার ক্ষেত্রেই থাকতে পারে। কিন্তু আমরা আমাদের জন্মদাতা নন, আমাদের পিতাকেই নির্দেশ করি পরিচয়দানের ক্ষেত্রে। আর পিতা সব সময় মায়ের বিবাহিত স্বামী। আমার জন্মদাতা আমারই পিতা কি না, এই ধরনের চিন্তায় দ্বারা বা অনুসন্ধানে নেমে সত্যকে আবিষ্কার করতে পারা বা না পারার মধ্যে কী আসে যায়?
ডা. রমাকাণ্ড কোনি প্রসঙ্গে বরং এবার আসা যাক। ডা. কোনির দাবির সমর্থনে প্রমাণ চেয়ে ’৮৪-র ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২৮ মার্চ দুটি চিঠি দিই। প্রথম চিঠিটি এখানে তুলে দিচ্ছি।
প্রবীর ঘোষ
৭২/৮, দেবীনিবাস রোড
কলকাতা-৭০০ ০৭৪
ডা. রমাকান্ত কোনি
বোধে হাসপাতাল
মেডিকেল রিসার্চ সেণ্টার
৩য় তল, বোম্বে-৪০০ ৫২০
প্রিয় ডা. কোনি,
সম্প্রতি আপনি, ভারতের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রচুর পাওয়া এক ‘ফেইথ হিলার’। আপনিও ফিলিপিনো ফেইথ হিলারদের মতোই দাবি করেন অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা বিদেহী ডাক্তারদের সাহায্যে রোগীদের রোগমুক্ত করেন।
আমার ধারণা, যে সব রোগীদের Placebo চিকিৎসার দ্বারা অর্থাৎ বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে রোগমুক্ত করা সম্ভব আপনি কেবলমাত্র তাঁদেরই বিনা ওষুধে রোগমুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন এবং হবেন। অথবা ‘বিদেহী ডাক্তার রোগীর প্রয়োজনীয় ওষুধের নাম লিখেছে’, দাবি করলেও বাস্তবে চিকিৎসা বিষয়ক জ্ঞানকে কাজে লাগিয়েই আপনি ব্যবস্থাপত্র লিখছেন। যে ব্যবস্থাপত্র অনুসারে চিকিৎসা করিয়ে রোগীরা রোগমুক্ত হচ্ছেন।
আপনি কি বাস্তবিকই দাবি করেন—বিদেহী ডাক্তারের আত্মাকে কাজে লাগিয়ে যে কোনও রোগীকে রোগমুক্ত করতে আপনি সক্ষম?
আমি অলৌকিক ক্ষমতা বিষয়ে জানতে আগ্রহী সত্যানুসন্ধানী। তথাকথিত অলৌকিকতার পিছনে লৌকিক রহস্য কী, এই বিষয়ে কিছু পত্র-পত্রিকায় লিখেও থাকি। দীর্ঘদিন ধরে বহু অনুসন্ধান চালিয়েও আজ পর্যন্ত একজন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারীর সন্ধান পাইনি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখেছি ওইসব তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারদের প্রত্যেকেরই ক্ষমতার পিছনে কোনও অলৌকিকত্ব ছিল না, ছিল লৌকিক কৌশল।
আমার এই ধরনের সত্যকে জানার সদিচ্ছা ও শ্রমকে নিশ্চয়ই আপনি একজন সৎ মানুষ হিসেবে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বাগত জানাবেন। আপনার অলৌকিক চিকিৎসা ক্ষমতার বিষয়ে আমি একটি অনুসন্ধান চালাতে চাই। আশা রাখি সত্য প্রকাশের স্বার্থে আপনি আমার সঙ্গে আন্তরিকতার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন।
আমি আপনার কাছে তিনজন রোগীকে হাজির করতে চাই। আপনার অলৌকিক ক্ষমতায় ওই তিনজনকে ছয় মাসের মধ্যে রোগমুক্ত করতে সক্ষম হলে আপনার অলৌকিক ক্ষমতাকে স্বীকার করে নিয়ে আপনাকে দেব দশ হাজার টাকা।
আপনি আমার সঙ্গে সহযোগিতা না করলে বা চিঠি পাঠাবার এক মাসের মধ্যে আমার সঙ্গে যোগাযোগ না করলে অবশ্যই ধরে নেব, আপনার দাবি একান্তই মিথ্যা। আপনি লৌকিক উপায়েই কিছু কিছু রোগীর রোগমুক্তি ঘটিয়ে থাকেন মাত্র।
শুভেচ্ছাসহ
প্রবীর ঘোষ
কোনি তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার বিষয়ে সত্যানুসন্ধানে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসেননি। কারণ এগিয়ে এসে পরাজিত হওয়ার চেয়ে এড়িয়ে যাওয়াকেই শ্রেয় মনে করেছিলেন, যেমন আরও অনেক ‘ক্ষমতাধরেরাই’ করেন।
ডাইনি সম্রাজ্ঞী ঈপ্সিতার ভূতুড়ে চিকিৎসা
১৯৮৮ সালটা যে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারিণীকে নিয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন পত্রিকাগুলো হইচই ফেলে দিয়েছিল তাঁর নাম ঈপ্সিতা রায় চক্রবর্তী, ডাইনি সম্রাজ্ঞী। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষাভাষী পত্র-পত্রিকায় রঙিন ও সাদা-কালো ছবির সঙ্গে যে সব প্রচ্ছদ কাহিনি ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল সে সব পড়ে পাঠক-পাঠিকারা শিহরিত হলেন। শিহরিত হলাম আমিও। জানলাম, রহস্যবিদ্যা ঈপ্সিতার মুঠোবন্দি। থট্ রিডিং বা মানুষের মন বোঝার ক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছেন সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী সাংবাদিকদের। নিখুঁত ভবিষ্যৎবাণী করতে সক্ষম। মারণ-উচাটন, তুকতাক সবই আয়ত্তে। ডাকিনী বিদ্যার সাহায্যে যে কোনও রোগীকে ইচ্ছে করলেই সুস্থ করে তুলতে পারেন, সে কোনও সুস্থ মানুষকে পারেন মারতে। ঈপ্সিতার দাবি, ডাইনির এইসব অলৌকিক ক্ষমতা বিজ্ঞানসম্মত সাধনার ফল। অলৌকিক ঘটনার প্রতি চিরকালই আমার আকর্ষণটা বড় বেশি। এই ধরনের কোনও ঘটনা শুনলে সত্যানুসন্ধানে নেমে পড়ার ইচ্ছেটা প্রবলতর হয়ে ওঠে। তার মধ্যে আবার, অলৌকিক ব্যাপার-স্যাপার যদি ‘বিজ্ঞানসাধনার ফল’ হয় তবে তো কথাই নেই। ঈন্সিতার ঘনিষ্ঠ এক সাংবাদিককে অনুরোধ করলাম আমার সঙ্গে ঈপ্সিতার পরিচয় করিয়ে দিতে। কয়েক দিনের মধ্যে খবর পেলাম, ঈপ্সিতা আমার মুখোমুখি হতে অনিচ্ছুক।
৮৮-র জুনের শেষ সপ্তাহে পড়ন্ত বিকেলে ইপ্সিতার দক্ষিণ কলকাতার লেক রোডের ছবির মতো সাজানো ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম ‘আজকাল’ পত্রিকার তরফ থেকে সাক্ষাৎকার নিতে। ঘরের দু’পাশে দুই বেড-ল্যাম্প সৃষ্ট আলো-আঁধারের মাঝে এক সময় ঈলিতার আবির্ভাব ঘটল। যথেষ্ট সময় ও যত্ন নিয়ে নিজেকে সাজিয়েছিলেন। আমি ও আমার সঙ্গী চিত্র-সাংবাদিক তাপস দেব পরিচয় দিলাম। ঈপ্সিতা বসলেন। আমার মিথ্যে পরিচয়কেই সত্যি বলে ধরে নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। সত্যানুসন্ধানে এসে প্রথম সত্যটি আমার সামনে প্রকাশিত হল, ঈপ্সিতার থট্ রিডিং ক্ষমতার দাবি নেহাতই বাত্কে-বাত্।
মণ্ট্রিয়লে শিক্ষা ও ডাইনি দীক্ষা পাওয়া ঈপ্সিতা ইংরেজির সঙ্গে কিছু কিছু বাংলা মিশেল দিয়ে জানালেন, তাঁদের সংস্থার নাম ‘ওয়ার্ল্ড উইচ ফেডারেশন’। কেন্দ্রীয় কার্যালয় মণ্ট্রিয়লে। সংস্থার তরফ থেকে পৃথিবীকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করে তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তিন প্রধানকে। এঁরাই সংস্থার সর্বোচ্চ পদাধিকারী। পূর্বাঞ্চলের কার্যালয় নিউ দিল্লি, প্রধানা স্বয়ং ঈন্সিতা। তবে ঈপ্সিতা যখন তাঁর কলকাতার ফ্ল্যাটে থাকেন তখন সেটাই হয়ে ওঠে অস্থায়ী কার্যালয়। ডাইনিপীঠের কেন্দ্রীয় সদস্য সংখ্যা মাত্র ৭৫ এবং সকলেই মহিলা।

অনেক পুরুষই সদস্য হওয়ার ব্যর্থ আবেদন রেখেছিলেন। আলোচনার মাঝে চা ও বিস্কুট এল। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বললাম, “কৈশোর থেকেই ওকাল্ট বা রহস্যবিদ্যার প্রতি একটা তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেছি। এ-জন্য ডাইনি, ডাইন, ওঝা, গুনিন, জানশুরু, তান্ত্রিক, ভৈরবী, অবতারদের পিছনে কম ঘুরিনি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই গাদা, সময় আর গুচ্ছের অর্থনাশই সার হয়েছে। যখন বাস্তবিকই সন্দেহ করতে শুরু করেছিলাম, এ জীবনে আর বোধহয় রহস্যবিদ্যার হদিশ দেওয়ার মতো কারও দেখা পেলাম না, এমনি সময় আপনার খোঁজ পেলাম। আপনাকে নিয়ে অন্তত গোটা আটেক লেখা আমার চোখে পড়েছে। সবই গোগ্রাসে গিলেছি। সব পড়ে সব জেনেও কেমন যেন বিশ্বাস করতে মন চাইছে না, তাই আমি নিজে আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাগুলোতে আপনার সম্বন্ধে যে সব আপাত অদ্ভূত খবর ছাপা হয়েছে তা সবই কি সত্যি?”
ঈপ্সিতা পরম অবহেলায় আমার দিকে তাকিয়ে ঠোঁটের ফাঁকে এক টুকরো অবজ্ঞার হাসি ঝুলিয়ে দিয়ে বললেন, “বাস্তবিকই প্রতিটি প্রকাশিত ঘটনাই সত্যি। এই তো গত ৬ জুন এক মাঝবয়সি ভদ্রলোক এসেছিলেন। নাম তারাকুমার মল্লিক। থাকেন এই কলকাতারই ৪৪ বি, রানি হর্ষমুখী রোডে। সমস্যাটি তারাকুমারবাবুর ভাগ্নী মঞ্জু চ্যাটার্জিকে নিয়ে। মঞ্জু রাতে এবং শয্যাক্ষতে শয্যাশায়ী। ডাক্তার ও হাসপাতাল ঘুরে এখন বাড়িতেই আছেন। এঁরা প্রত্যেকেই জবাব দিয়েছেন। শয্যাক্ষতের তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করার ক্ষমতাও হারাতে বসেছেন মঞ্জু। সঙ্গে উপসর্গ অনিদ্রা। কসমিক-রে চার্জ করা জলে ডাইনি শক্তি মিশিয়ে এক শিশি তারাকুমারকে দিয়ে মঞ্জুর শরীরে লাগাতে বলেছিলাম। এক সপ্তাহেই দারুণ ফল পাওয়া গেল। ১৩ তারিখ তারাকুমার জানালেন মঞ্জুর শরীরের শয্যাক্ষতের জ্বালা-যন্ত্রণা অনেক কম।”
না বুঝেও ‘বুঝেছি’ ভান করা আমার ধাতে সয় না। তাই অকপটে ঈপ্সিতাকে জানালাম, কসমিক-রে চার্জের ব্যাপারটা মাথায় ঢোকেনি।
ঈপ্সিতা যথেষ্ট যত্ন সহকারে বিষয়টা বোঝালেন। জানালেন, তাঁদের সংস্থার তিন প্রধানের কাছে তিনটি ক্রিস্টাল-বাটি আছে। ক্রিস্টালের বাটিতে জল, লাল গোলাপের পাপড়ি, কিছু বিভিন্ন ধরনের বিশেষ রত্ন পাথর, রুপোর টুকরো এবং সেণ্ট ঢেলে বাটিটি রোদে রাখেন। বাটির এমনই গুণ, সেটা সূর্য রশ্মি থেকে কসমিক-রে শোষণ করে জলে জমা করে। ঈপ্সিতার কথায়, এটা ম্যাগনেটাইজড্ জল। এই ম্যাগনেটাইজড্ জলে হাত ডুবিয়ে ঈপ্সিতা তাঁর মানসিক শক্তি জলে মিশিয়ে দেন।
আবার ধাক্কা খেলাম, ঈপ্সিতার বিজ্ঞান বিষয়ে সাধারণ জ্ঞানটুকুরও অভাব দেখে। কসমিক-রে বা মহাজাগতিক রশ্মি শক্তিশালী তড়িৎকণার বিকিরণ। এই অদৃশ্য তড়িৎকণার বিকিরণ সারা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত। সেই সন্ধ্যায় ঈন্সিতা আমার হাতে যে চারের পেয়ালা তুলে দিয়েছিলেন, তাতেও ছিল কসমিক-রে। আসলে অজ্ঞানতার দরুন ঈপ্সিতা সূর্য-রশ্মি ও মহাজগতিক রশ্মিকে গুলিয়ে ফেলে নিজের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে এক অদ্ভুত তথ্য তৈরি করেছিলেন। ঈন্সিতার দৌড় আরও যতটুকু সম্ভব বোঝার তাগিদে কসমিক-রে নিয়ে তাঁর ভ্রান্ত ধারণার প্রসঙ্গ না তুলে ঈপ্সিতাকে বক্বক্ করে যাওয়ার সুযোগ দিলাম।
ঈপ্সিতা বলে চললেন, ডাইনি বিদ্যাকে বলা হয় রহস্যবিদ্যা বা অপরসায়ন। মজা হল, আমাদের এই অলৌকিক রহস্যবিদ্যা বা অপরসায়নের তথাকথিত অবৈজ্ঞানিক কাণ্ড-কারখানাগুলো আমরা ঘটিয়ে চলেছি বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই। এই যে ৪৯টি মহাজাগতিক রশ্মি সূর্যের আলো থেকে আমরা গ্রহণ করছি, এই ৪৯টি মহাজাগতিক রশ্মির কথা তথাকথিত বিজ্ঞানের অগ্রগতির অনেক অনেক আগে ঋকবেদেই লেখা রয়েছে। এমনিভাবেই আমরা অপরসায়নের জ্ঞান অর্জন করেছি ইহুদিদের কোবলা, মিশরীয়দের অপদেবী আইসিসের আরাধনা সংক্রান্ত, বই, ‘দ্য কিং অফ্ সলোমন’, তিব্বতের তন্ত্র ইত্যাদি পড়ে।
পৃথিবীর সব কিছুর মধ্যেই রয়েছে পাঁচটি মৌল শক্তি—মাটি, জ্বল, আগুন, হাওয়া ও আকাশ বা মহাশূন্য। এই মৌল শক্তিগুলো থেকেই আমরা বিশেষ ডাইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয় করি। তারপর তার সঙ্গে যখন আমাদের মানসিক শক্তিকে মিলিয়ে দিই, তখন যে ক্ষমতা আমাদের মধ্যে আসে, সেটাকেই সাধারণ মানুষে বলেন অলৌকিক ক্ষমতা।
অজ্ঞানের কাছে বিজ্ঞানের কথা শুনতে শুনতে ক্লান্ত লাগছিল। বললাম, “আপনাদের ডাইনিবিদ্যা কেমনভাবে শেখানো হয় এই প্রসঙ্গে আপনার বক্তব্য বলে কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, শিক্ষাক্রমের প্রথম চার বছর বিভিন্ন প্রাচীন পুঁথিপত্র পড়ে অপরসায়ন বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করতে হয়। পরবর্তী দু’বছর আপনারা শেখেন মনকে শক্ত করে তৈরি করতে। এই সময় আপনারা বহু পুরুষকে ভালোবাসেন, কিন্তু হৃদয় অর্পণ করেন না, বহু পুরুষদের সঙ্গ দেন আবার যখন ইচ্ছে তাঁদের ছেঁড়া কাগজের মতোই ছুঁড়ে ফেলে দেন। এসব কি বাস্তবিকই আপনাদের ডাইনি হওয়ার শিক্ষাপদ্ধতির অঙ্গ, না কি এই ধরনের নীতিহীন, মূল্যবোধহীন, অফ্ বিট্ কিছু বলে প্রচারের মধ্যে আসতে চেয়েছিলেন।”
ঈপ্সিতার চোখ সরু হল, সম্ভবত ঘাড়টা শক্ত হল। “যা সত্য, সেটুকুই বলেছি। কার কাছে আমার বক্তব্য অফ্ বিট্ মনে হবে, কার কাছে হবে না, সেটা আমার বিবেচ্য নয়।”
“আপনার মেয়ে দীপ্তার বয়স এখন বছর দশেক। তাকে আপনি না কি ডাইনি করে তুলছেন। আপনার কিশোরী কন্যা যখন আপনারই চোখের সামনে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করবে তখন কি তা স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারবেন?”
“না পারার কী আছে? ওটা তো মনকে শক্ত করে তৈরি করার একটা পরীক্ষা মাত্র”, বললেন ঈপ্সিতা।
ঈপ্সিতার মানসিক স্বাভাবিকত্ব নিয়ে একটা সন্দেহ তীব্র হল।
বললাম, “সানন্দা’র শংকরলাল ভট্টাচার্যকে আপনি আপনার অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছিলেন বলে পড়েছি। আপনার অলৌকিক ক্ষমতা নিজের চোখে দেখার প্রচণ্ড ইচ্ছে নিয়ে এসেছি। একান্ত অনুরোধ, বিফল করবেন না।”
ঈপ্সিতা আমার অনুরোধে আফ্রিকার ভুডু মন্ত্রের সাহায্যে একটা ঘটনা ঘটিয়ে দেখাতে রাজি হলেন। জানালেন, এই ধরনের অনুরোধ রেখেছিলেন টাইম্স্ অফ্ ইণ্ডিয়ার শিখা বসু। তাঁকে ভুডু মন্ত্রে যা ঘটিয়ে দেখিয়েছিলেন তাই দেখে শিখা ও তাঁর চিত্রসাংবাদিক সঙ্গী মোনা চৌধুরী প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ঈপ্সিতা আরও বললেন, “দেখি আপনার এবং আপনার সঙ্গীর নার্ভ কত শক্ত।”
ঈপ্সিতা উঠে ভিতরের ঘরে চলে গেলেন। এলেন একটি পুতুল নিয়ে। পুতুলের উচ্চতা দেড় ফুটের মতো। পরনে প্যাণ্ট, শার্ট, টাই, কোট, হ্যাট। মুখটা কাঠের, কালো রঙের পালিশ করা। ঈন্সিতার সঙ্গী এবার মেয়ে দীপ্তা। ওর হাতে একটা ট্রে। তাতে তিনটি বেগুন। আমার সঙ্গী তাপস ছবি তোলা শুরু করল। ঈন্সিতা তাঁর হাতের পুতুলটা তুলে ধরে বললেন, “এটাই ভুডু। জীবন্ত প্রেতাত্মা।”
ঘরের লাগোয়া ঘেরা বারান্দায় একটা টেবিল। দু’পাশে দুটো চেয়ার। টেবিলের পাশেই একটা দামী টুল। তার উপর ভুডু মূর্তিটিকে নামিয়ে রাখলেন ঈপ্সিতা। দীপ্তা তার হাতের ট্রেটা নামাল টেবিলে। ঈপ্সিতা তাঁর দু’হাতের দশ আঙুলকে কাজে লাগিয়ে চুলগুলোকে এলো করে ছড়িয়ে দিলেন। দু’হাতের তালুতে গোলা সিঁদুর ঘষলেন। কপালেও লাগালেন গোলা সিঁদুরের টিপ। দীপ্তা ঘরের ভিতরে গিয়ে নিয়ে এল দুটো মাটির ভাঁড়।
ঈপ্সিতা ভুডু মূর্তিটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিড় বিড় করে কী সব মন্ত্র পড়তে পড়তে ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাতে লাগলেন। এক সময় আমাকে অনুরোধ করলেন ট্রে থেকে একটা বেগুন তুলে ওঁর হাতে দিতে। দিলাম। ঈপ্সিতা একটা চেয়ারে বসলেন। ঈন্সিতার কথা মতো মুখোমুখি চেয়ারটায় বসলাম আমি। টেবিলের উপর একটা মাটির ভাঁড় বসিয়ে তার উপর বেগুনটাকে বসালেন। আর একটা মাটির ভাঁড় উপুড় করলেন বেগুনটার মাথায়। এ-বার ঈপ্সিতা আমার চোখে চোখ রেখে বললেন, “আপনার কোনও শত্রু আছে?”
বললাম, “থাকতে পারেন, আবার নাও থাকতে পারেন।”
ঈপ্সিতা বললেন, “এখন আমরা ভুডু মন্ত্রের চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পড়েছি। আপনার কোনও শত্রু থাকলে তার নাম বলুন। জীবন্ত প্রেতাত্মাকে স্মরণ করে বেগুনটা কেটে ফেলব, অমনি দেখতে পাবেন বেগুনের কাটা অংশে রক্তের দাগ। রক্তের দাগ যত তীব্র হবে, শত্রুর শারীরিক ক্ষতিও ততই তীব্র হবে। ভুভু মন্ত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে বেগুনের পরিবর্তে চিচিঙা বা পাতিলেবুও ব্যবহৃত হয়।”
বললাম, “সবই তো বুঝলাম। কিন্তু আমার কোনও শত্রু নেই। তামি নির্বিরোধী ছাপোষা কলমচী মাত্র।”
“বেশ তো আমরা বরং একটা মানসিক শক্তির পরীক্ষা করে দেখি। আপনি আপনার সমস্ত মানসিক শক্তি দিয়ে ভাবতে থাকুন বেগুনটার ভেতর যেন সাদাই থাকে। আমি আমার মানসিক শক্তিকে অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে বেগুনটার ভেতর মানুষের রক্ত নিয়ে আসতে চেষ্টা করব।” বললেন ঈপ্সিতা।
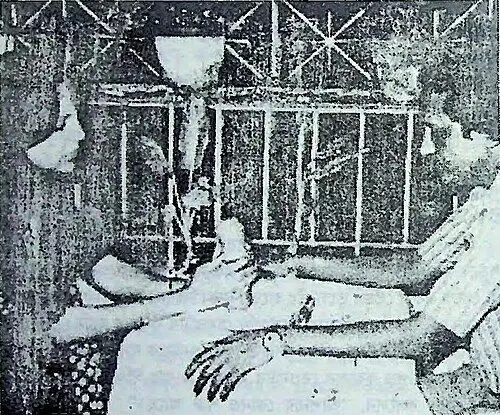
দু’জনে কিছুক্ষণ মুখোমুখি বসে বেগুনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এক সময় ঈপ্সিতা বললেন, “দেখি আপনার নাড়ির গতি।” আমার নাড়ির গতি পরীক্ষা করে বললেন, “স্বাভাবিকই আছে দেখছি। আপনার নার্ভের তারিফ করতেই হবে। আপনি এক মনে ভাবতে থাকুন বেগুনের ভেতরটা সাদাই আছে। যখন আপনার মনে হবে বাস্তবিকই বেগুনটা সাদাই আছে, তখন আমাকে বলবেন। বেগুনটা কাটব।”
আমি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বললাম, “এবার কাটুন।”
ঈপিতা তাঁর ডাইনি ছুরি ‘ড্যাগার অফ জাস্টিস’ তুলে বেগুনটা কেটে ফেললেন। বেগুনের ভিতরের সাদা অংশের খানিকটা জায়গা টকটকে লাল রক্তে ভেজা।
ঈপ্সিতা উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, “দেখছেন রক্ত। এটা আপনার অজ্ঞাত শত্রুর রক্ত।”
বেগুনের টুকরো দুটো হাতে নিয়ে এক মুহূর্ত পরীক্ষা করে বিনীতভাবে জানতে চাইলাম, “আপনি কী ভাবে ঘটালেন?”
“ভুডু মন্ত্রে। এই পদ্ধতিতে পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তের শত্রুকেই বধ করতে পারি আমরা।”
বললাম, “ঈপ্সিতা, ট্রে থেকে যে কোনও একটা বেগুন আমার হাতে তুলে দিন। তারপর আপনি আপনার সমস্ত ইচ্ছে শক্তি দিয়ে চেষ্টা করুন বেগুনটার ভেতরটা সাদা রাখতে। আমি কোনও মন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই বেগুনটা কেটে রক্ত বের করে দেব, ফোনটি আপনি করলেন।”
আমার কথা শুনে ঈপ্সিতার মুখের চেহারা গেল পাল্টে। তবু প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে শক্ত মাটিতে শেষ বারের মতো দাঁড় করাতে চাইলেন। বললেন, “ওইসব ছেলেমানুষি চিন্তা মাথায় রাখবেন না। ভুডু মন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ জানাবার ফল প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভয়াবহ।”
বললাম, “কোনও ভয় নেই আপনার। আমার কোনও ক্ষতির জন্য আপনাকে সামান্যতম দোষারোপ করব না। আপনি আমার হাতে একটা বেগুন তুলে দিন।”
উত্তেজিত, শঙ্কিত ঈপ্সিতা দীপ্তার হাতে ট্রেটা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, “এটা ভেতরে নিয়ে যাও।”
দীপ্তাকেও যথেষ্ট নার্ভাস মনে হচ্ছিল। ও দ্রুত আদেশ পালন করল। আমি নিশ্চিত ছিলাম, প্রতিটি বেগুনেই লাল তরল ঢোকানো আছে। অথবা ছুরিতে মাখানো আছে রসায়ন। ঈন্সিতাকে আরও একটা চমক দিতে বললাম, “আমারও কিছু ক্ষমতা আছে।”
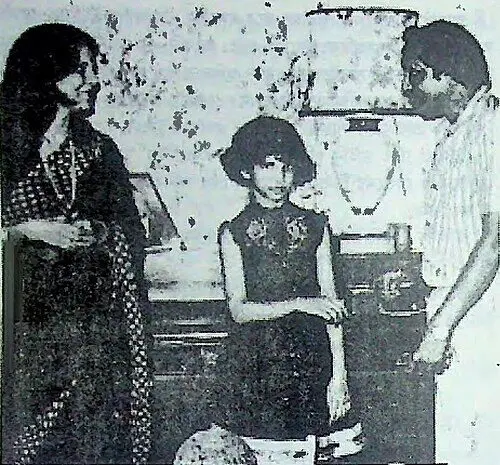
ঈপ্সিতা সন্দেহজনক চোখে তাকালেন। লৌকিক কৌশলে তথাকথিত কয়েকটি অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে দেখানোতে ঈপ্সিতা ভাবাবেগে আপ্লুত হলেন, উচ্ছ্বসিত হলেন। বললেন, “আপনি জানেন না, ঠিক বুঝতে পারছেন না, আপনার কী প্রচণ্ড রকম অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে। এই ক্ষমতাকে ঠিক মতো ব্যবহার করতে পারলে দুনিয়া জুড়ে হইচই পড়ে যাবে। ওয়ার্ল্ড উইচ একজিকিউটিভ কমিটির সভ্য হওয়ার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনিই হলেন পৃথিবীর প্রথম পুরুষ মানুষ যিনি এই আমন্ত্রণ পেলেন। আপনাকে এই দূর্লভ সম্মান জানানোর কারণ, আপনার কাছ থেকে আমাদেরও অনেক কিছু শেখার আছে।”
ঈপ্সিতার উচ্ছ্বাস আমার মধ্যে সংক্রামিত না হওয়ায়, তার মতো রমণীয় রমণীর আমন্ত্রণ গ্রহণ না করায় তিনি যেমন অবাক হয়েছিলেন তেমনই নিরাশ। শেষ চেষ্টা হিসেবে আমন্ত্রণ জানালেন শনিবার দুপুরের আগে আসার। আরও কিছু না কি বলার আছে। শনিবার গিয়েছিলাম তাপসকে নিয়েই। নিষ্ফল কিছু কথাবার্তার মধ্যে আমার সফলতা ছিল একটিই। ঈপ্সিতা পরম ভালোবেসে একটি সুন্দর আধারে দিলেন ম্যাগনেটাইজড জল।
৮ জুলাই বিকেলে গিয়েছিলাম মঞ্জু চ্যাটার্জির বাড়িতে। মধ্য বয়সি মঞ্জুকে দেখলাম শয্যাক্ষতে শয্যাশায়ী। শয্যাক্ষতের তীব্র গন্ধে বাতাস ভারী। কথা বললাম মঞ্জুর মা শান্তি সেন এবং সেবার দায়িত্বে নিয়োজিত মীরা দাসের সঙ্গে। তিনজনই জানালেন, বাস্তবিকই দীর্ঘ চিকিৎসার পর ইন্সিতার কসমিক-রে চার্জ করা অলৌকিক জল প্রতিদিন শরীরে বুলিয়ে ভালোই ফল পাচ্ছিলেন। শরীরের জ্বালা-যন্ত্রণা কিছুটা কম ছিল। শেষ শনিবার মন্ত্রপূতঃ জল না নিয়েই ফিরেছিলেন। তারপর থেকে যন্ত্রণাটা আবার তীব্র আকার ধারণ করেছে। ঘুম আসছে না। মঞ্জু কথা বলতে বলতে কাঁদছিলেন। আমি ঈপ্সিতার কাছ থেকে আসছি শুনে মঞ্জু অনুরোধ করলেন, “আপনি একটা কিছু করুন। এই যন্ত্রণা আমি আর সহ্য করতে পারছি না।”
মঞ্জুর উপর একটা পরীক্ষা চালাতে চাইলাম। মঞ্জুকে বললাম, “আমি কিছু কথা বলব, কথাগুলো আপনি চোখ বুজে মন দিয়ে শুনুন। আপনার যন্ত্রণা কমে যাবে, ভালো লাগবে, ঘুম হবে।” শান্তি দেবী ও মীরার উপস্থিতিতেই ‘হিপনটিক সাজেশন’ দিলাম। মিনিট দশ-পনেরো সাজেশন দেওয়ার পর মঞ্জুকে জিজ্ঞেস করলাম, “কেমন লাগছে?”
মঞ্জু বললেন, “ভালো লাগছে। ব্যথা-যন্ত্রণা অনেক কমে গেছে। আমার ঘুম পাচ্ছে।”
বললাম, “ঘুমান। আমি আবার পরশু সকালে এগারোটা নাগাদ এসে খবর নেব, কেমন ছিলেন।”
রবিবার সাড়ে বারোটা নাগাদ গিয়েছিলাম। গিয়েই একটা আশ্চর্য খবর শুনলাম। ঈপ্সিতা এসেছিলেন। সাড়ে দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত মঞ্জুর ঘরে ছিলেন।
ডাইনি সম্রাজ্ঞী ঈপ্সিতা হঠাৎ প্রথা ভেঙে বৈভব ছেড়ে গরিবের ভাঙা ঘরে এসেছিলেন কি শুধুই আর্তের সেবায়? তারাকুমারের কথাতেই আমার প্রশ্নের উত্তর পেলাম। শনিবার তারাকুমারের কাছে আমার আগমন বার্তা ও মঞ্জুর অবস্থার পরিবর্তনের কথা ঈন্সিতা শুনেছেন। আরও জেনেছিলেন আমি রবিবার এগারোটা নাগাদ আবার আসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।
মঞ্জু, শান্তি দেবী, মীরা এবং তারাকুমারবাবুর সঙ্গে মঞ্জুর বর্তমান অবস্থা নিয়ে কথা হল। চারজনই জানালেন আমার কথাগুলো শোনার পর মঞ্জু দেবীর যন্ত্রণা অনেক কম অনুভূত হচ্ছে। ঘুমও ভালো হচ্ছে। এ-বাড়ির প্রত্যেকের কথাগুলো ধরে রাখলাম টেপ রেকর্ডারে। বিদায় নেওয়ার সময় ওঁরা আবার আসার আমন্ত্রণ জানালেন।
মঞ্জুর উপর পরীক্ষা চালিয়ে আমি যা জানতে চেয়েছিলাম, তা জানতে পেরে খুশি হলাম। ঈপ্সিতা মঞ্জুর বিশ্বাসবোধকে কাজে লাগিয়েই মঞ্জুর যন্ত্রণা সাময়িকভাবে কিছুটা কমাতে পারেন। এই ধরনের যন্ত্রণা কমার কারণ কখনই ঈপ্সিতার অলৌকিক ক্ষমতা নয়, এর কারণ রয়ে গেছে লৌকিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মধ্যে। বিশ্বাস-নির্ভর এই ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতিকে বলে ‘প্ল্যাসিবো’ (Placebo) চিকিৎসা পদ্ধতি। এ বিষয়ে আগে বিস্তৃতই আলোচনা করেছি। যাঁরা এইসব অলৌকিক উপায়ে রোগমুক্ত হয়েছেন খোঁজ নিলেই দেখতে পাবেন তাঁরা প্রত্যেকেই সেই সব অসুখেই ভুগছিলেন, যে সব অসুখ বিশ্বাসে সারে। ঈপ্সিতা কাদের রোগমুক্ত করবেন তা ছিল সম্পূর্ণই ঈন্সিতার ইচ্ছাধীন। নিজের ইচ্ছেমতো রোগী নির্বাচনের দায়িত্ব রাখার কারণ তিনি সেইসব রোগীদেরই বাছতেন যাদের প্ল্যাসিবো চিকিৎসায় ভালো হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
ঈপ্সিতার কাছ থেকে আমি যে অলৌকিক জল সংগ্রহ করেছিলাম, তা পরীক্ষার জন্য তুলে দিয়েছিলাম রসায়ন বিজ্ঞানী ড. শ্যামল রায়চৌধুরীর হাতে। ড. রায়চৌধুরী কিন্তু ওই অপার্থিব জলে পার্থিব স্টেরয়েড-এর অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছিলেন। এরপর এই সত্যটুকু আবিষ্কার করে আরও এক দফা বিস্মিত হলাম। ঈপ্সিতার নিজের ওপরই নিজের ভরসা নেই, তাই তাঁকে নির্ভর করতে হয়েছে স্টেরয়েডের উপর।
১২ আগস্ট ‘আজকাল’ পত্রিকায় ঈন্সিতাকে নিয়ে আমার একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে এই ঘটনারই সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হয়েছিল। শেষ অনুচ্ছেদে লিখেছিলাম, ‘ঈপ্সিতা কি তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ রাখতে আমার হাজির করা পাঁচজন রোগীকে সুস্থ করে তুলতে রাজি আছেন? তিনি জিতলে আমি দেব পঞ্চাশ হাজার টাকার প্রণামী, সেই সঙ্গে থাকব চিরকাল তাঁর গোলাম হয়ে।’
১৩ আগস্টের আর একটি ঘটনার উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। সে-রাতের লালগোলা প্যাসেঞ্জারে বহরমপুর যেতে হয়েছিল পুলিশ দেহরক্ষী নিয়ে। কারণ—‘আজকাল’ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅশোক দাশগুপ্তের কাছে একটি খবর এসেছিল-সে রাতে আমার কম্পার্টমেণ্টে ডাকাত পড়বে। ডাকাতির আসল উদ্দেশ্য আমাকে হত্যা করা। অর্থাৎ, হত্যার উদ্দেশ্য গোপন রাখতে ডাকাতির অভিনয় হবে। খবর ছিল ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ প্রেসিডেন্সি রেঞ্জ মিস্টার সুফির কাছেও। তারই পরিপ্রেক্ষিতে দেহরক্ষীর ব্যবস্থা।
১১ ডিসেম্বর ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির ডাকা সাংবাদিক সম্মেলনে ডাইনি সম্রাজ্ঞী ঈপ্সিতাকে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা প্রমাণ করার জন্য সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলাম ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির পক্ষে। ঈপ্সিতা চিঠিটা স্বয়ং গ্রহণ করলেও চ্যালেঞ্জ গ্রহণের মতো সততা, সাহসিকতা বা ধৃষ্টতা দেখাননি। যদি দেখাতেন তবে অবশ্যই তাঁর মাথা যুক্তিবাদী আন্দোলনের কাছে, বিজ্ঞানের কাছে নতজানু হতই। তিনি অবশ্যই সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে চূড়ান্তভাবে বিধ্বস্ত হওয়ার চেয়ে উপস্থিত না হওয়াকেই শ্রেয় ও কম-তাপমানজনক মনে করেছিলেন।
ডাইনি সম্রাজ্ঞীর কাছে সমিতির পক্ষ থেকে সমিতির প্যাডে যে চিঠি পাঠিয়েছিলাম আপনাদের কৌতূহল মেটাতে তা এখানে তুলে দিলাম:
ঈন্সিতা রায় চক্রবর্তী
৬৪, লেক রোড,
ফ্ল্যাট ২ এম, ডব্লিউ, ‘বলাকা বিল্ডিং’,
কলকাতা – ৭০০ ০২৯
৫.১২.৮৮
মহাশয়া,
সাম্প্রতিককালে আপনিই সম্ভবত ভারতের সবচেয়ে প্রচার পাওয়া মানুষ। বিভিন্ন ভাষা-ভাষী পত্র-পত্রিকায় আপনার অলৌকিক ক্ষমতার বিষয়ে পড়েছি। কয়েক মাস আগের এক সন্ধ্যায় আপনারই ফ্ল্যাটে বসে আপনি আপনার অলৌকিক ক্ষমতার বিষয়ে অনেক কিছুই আমাকে বলেছিলেন। পড়েছি এবং শুনেছি, আপনি যে কোনও রোগীকে আপনার অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতার দ্বারা রোগ মুক্ত করতে পারেন। যে কোনও অপিরিচিত মানুষের অতীত ও ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন।
আমি অলৌকিক ক্ষমতা বিষয়ে জানতে আগ্রহী এক সত্যানুসন্ধানী। দীর্ঘ দিন ধরে বহু অনুসন্ধান চালিয়েও আজ পর্যন্ত একজনও অলৌকিক ক্ষমতাবান ব্যক্তি বা একটিও অলৌকিক ঘটনার সন্ধান পাইনি। আমার এই ধরনের সত্যানুসন্ধানের প্রয়াসকে প্রতিটি সৎ মানুষের মতোই আপনিও স্বাগত জানাবেন আশা রাখি। সেই সঙ্গে এও আশা রাখি, আপনার অলৌকিক ক্ষমতার বিষয়ে অনুসন্ধানে আপনি আমার সঙ্গে সমস্ত রকম সহযোগিতা করবেন।
আগামী এক মাসের মধ্যে আপনার সঙ্গে ঠিক করে নেওয়া কোনও একটি দিনে সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের উপস্থিতিতে আপনার সামনে হাজির করব পাঁচজন মানুষ ও পাঁচজন রোগীকে। পাঁচজন মানুষের অতীত সম্পর্কে সে-দিনই আপনাকে কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। পাঁচজন রোগীকে আপনার অলৌকিক ক্ষমতায় রোগ মুক্ত করার জন্য দেব ছয়মাস সময়। পরীক্ষা দুটিতে আপনি কৃতকার্য হলে আপনার অলৌকিক ক্ষমতা স্বীকার করে নেব আমি এবং ‘ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি।’ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রইলাম, আপনার অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ পেলে দেব পঞ্চাশ হাজার টাকা।
আমার সঙ্গে এই অনুসন্ধান বিষয়ে সহযোগিতা না করলে অবশ্যই ধরে নেব, আপনার সম্বন্ধে প্রচলিত প্রতিটি অলৌকিক কাহিনিই মিথ্যা।
আগামী ১১ ডিসেম্বর ৮৮ রবিবার বিকেল চারটের সময় আমাদের ময়দান তাঁবুতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আহ্বান করেছে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি। সে-দিন আপনাকে ওই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে আহ্বান জানাচ্ছি।
শুভেচ্ছাসহ—
প্রবীর ঘোষ।
ইপ্সিতার এই পলায়নী মনোবৃত্তিকে পরাজয়েরই নামান্তর ধরে নিয়ে শহর কলকাতা থেকে প্রকাশিত প্রতিটি নামী-দামি, বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকা প্রচণ্ড গুরুত্ব দিয়ে বিশাল আকারে খবরটি পরিবেশন করে। একাধিক দৈনিকে প্রকাশিত হয় দীর্ঘ সম্পাদকীয়। বহু পত্রিকা প্রকাশ করেছিল, সাংবাদিক সম্মেলনে সমিতির দামাল ছেলেদের ঘটানো অনেক অলৌকিক ঘটনার ছবি।
১১ ডিসেম্বর ’৮৮-র ঐতিহাসিক সাংবাদিক সম্মেলনে ডাইনী সম্রাজ্ঞী ইপ্সিতা ছাড়াও আহ্বান জানানো হয়েছিল আরও দুজনকে। তাঁরা হলেন, ‘শিক্ষা আশ্রম ইণ্টারন্যাশনাল’-এর সাঁই শিষ্য উপাচার্য ও হস্তরেখাবিদ নরেন্দ্রনাথ মাহাতো।
উপাচার্য ও শ্রীমাহাতো সরাসরি আমাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। আমাদের সমিতির পক্ষ থেকে সেই চ্যালেঞ্জ সানন্দে গ্রহণ করে চিঠি দিই ও তাঁদের ওই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে আমন্ত্রণ জানাই। উপাচার্যের চ্যালেঞ্জটি ছিল খুবই কৌতূহল জাগানো। তিনি জানিয়েছিলেন, স্রেফ সাঁইবাবার বিভূতি খাইয়ে সাঁইবাবার অপার অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ দেবেন। বিভূতি খাওয়ার তিন দিনের মধ্যে আমার পেটে তৈরি হবে ছয় থেকে এগারোটি স্বর্ণমুদ্রা। চতুর্থ দিন অপারেশন করলেই ওগুলো পেট থেকে হাতের মুঠোয় চলে আসবে।
তারপর যা যা ঘটেছিল, সে এক রোমাঞ্চকর কাহিনি। কিন্তু সে কাহিনি এখানে আনলে ‘ধান ভানতে শিবের গান’ গাওয়া হয়ে যাবে। এমনই আরও অনেক চ্যালেঞ্জারদের চ্যালেঞ্জে বহু রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছি, হয়েই চলেছি। কিন্তু সে-সব অভিজ্ঞতার কাহিনি ‘অলৌকিক নয়, লৌকিক’ বইতে আনা প্রাসঙ্গিক মনে হয়নি। যে-গুলো প্রাসঙ্গিকভাবে প্রথম খণ্ডে হয়তো আসতে পারত, সে সব চ্যালেঞ্জারদের অনেকেরই মুখোমুখি হয়েছি প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হবার পর। উৎসাহী পাঠক-পাঠিকাদের পিপাসা মেটাতে তাঁদেরই জন্য ‘যুক্তিবাদীর চ্যালেঞ্জাররা’ শিরোনামে একটা বই লেখায় মন দিয়েছি।