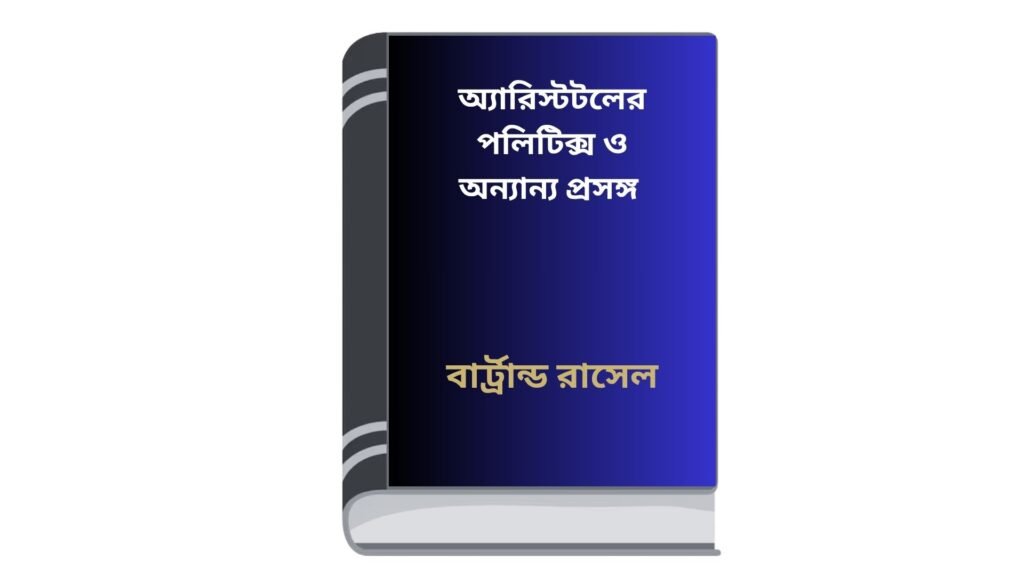৫. পদার্থবিজ্ঞান
৫. পদার্থবিজ্ঞান
অ্যারিস্টটলের দুটি বই এই অধ্যায়ের বিবেচ্য। একটির নাম Physics অন্যটি On the Heavens। বই দুটি পরস্পর নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। প্রথম বইটিতে আলোচনা যেখানে থেমেছে, দ্বিতীয় বইটি সেখান থেকে আলোচনা শুরু করেছে। দুটি বই-ই অত্যন্ত প্রভাবসম্পন্ন ছিল। গ্যালিলিও-এর যুগ পর্যন্ত এই দুটো বই বিজ্ঞানে কর্তৃত্ব করেছে। এই দুটো বইয়ে আলোচিত মতবাদগুলো থেকেই প্রতিমূর্তি বা উৎকৃষ্ট নিদর্শন ও পার্থিব-এর মতো শব্দাবলির উদ্ভব ঘটেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে এ দুটি বইয়ের কোনো বাক্য গ্রহণযোগ্য না হলেও দর্শনের ইতিহাসকারদের জন্য বই দুটো পাঠ করা আবশ্যক।
অধিকাংশ গ্রিকের মতো পদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের অভিমতগুলো বুঝতে তাদের কল্পনাপ্রবণ পশ্চাৎপট বুঝতে হবে। প্রত্যেক দার্শনিক জগতের আকার সম্পর্কে যে তত্ত্ব উপস্থাপন করেন তা ছাড়াও একটি বেশ সরল তত্ত্ব থাকে। এ সম্পর্কে তিনি বেশ অনবহিত হতে পারেন। যদি তিনি তা সম্পর্কে অবগত হয়ে থাকেন তাহলে তিনি সম্ভবত উপলব্ধি করতে পারেন যে ওই সরল তত্ত্বটি দিয়ে কাজ চলবে না। তাই তিনি তা লুকিয়ে রাখেন এবং এমন কিছু উপস্থাপন করেন যা অধিকতর সূক্ষ্ম। এই সূক্ষ্ম তত্ত্বটি তিনি বিশ্বাস করেন কারণ তা তার ওই কাঁচা তত্ত্বটির মতোই। কিন্তু ওই কাঁচা তত্ত্বটি তিনি এমনভাবে বিকশিত করেছেন, সূক্ষ্ম করে তুলেছেন যা ভুল প্রমাণিত করা যাবে না বলে তিনি মনে করেন। এ কারণেই তিনি তার তত্ত্বটিকে অন্যদের গ্রহণ করতে আহ্বান জানান। তত্ত্বটিতে এই সূক্ষ্মতা আসে নিরাকরণ পদ্ধতি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে; কিন্তু শুধু এই পদ্ধতি থেকেই কখনো ইতিবাচক ফল আসে না। পদ্ধতিটি সর্বোত্তম যা করতে পারে তা হলো এই যে, একটি তত্ত্ব সত্য হতে পারে, কিন্তু অবশ্যই সত্য হবে তা নয়। ইতিবাচক ফলটি আসে দার্শনিকের কল্পনাশ্রয়ী পূর্ব ধারণাগুলো থেকে বা Santayana যেটাকে জৈবিক বিশ্বাস বলেছেন, তা থেকে। দার্শনিকরা এটা তেমন উপলব্ধি করেন না, কিন্তু এ রকমই হয়।
পদার্থবিজ্ঞানের ব্যাপারে অ্যারিস্টটলের কল্পনাপ্রবণ পটভূমি একজন আধুনিক শিক্ষার্থীর চেয়ে খুবই ভিন্ন ছিল। বর্তমানকালে একটি বালক আরম্ভ করে বলবিদ্যা দিয়ে আর বলবিদ্যা নামটি থেকেই বোঝা যায় এর সঙ্গে জড়িত আছে যন্ত্রপাতি। আজকের বালক মোটর গাড়ি ও উড়োজাহাজের সঙ্গে খুব ভালোভাবে পরিচিত। অবচেতন কল্পনার সামান্যতম অবকাশেও সে মনে করে না যে মোটর গাড়ির ভেতরে কোনো একধরনের ঘোড়া আছে বা মনে করে না যে উড়োজাহাজের পাখায় পাখির পাখার মতো চমৎকার ক্ষমতা আছে। যে বিশ্বে মূলত প্রাণহীন ও তার সহায়ক একটি বস্তুগত পরিবেশের প্রভু হিসেবে মানুষ অপেক্ষাকৃত একা, সেই বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের কল্পিত ছবিগুলোতে পশু-প্রাণীর গুরুত্ব হারিয়ে গেছে। গ্রিকদের ক্ষেত্রে গতি সম্পর্কে কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাদানের বেলায় পুরোপুরি যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বলতে গেলে নেই। ডেমোক্রিটাস ও আর্কিমিডিসের মতো অল্পসংখ্যক প্রতিভাবান মানুষের ক্ষেত্রেই শুধু এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম দেখা গেছে। গ্রিকদের কাছে দুই ধরনের প্রপঞ্চ গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে মনে হয়। একটি হলো পশুদের চলাফেরা, অন্যটি গ্রহ-নক্ষত্রের চলাফেরা। একজন আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের কাছে একটি পশুর দেহ হলো অতিশয় জটিল ভৌত রাসায়নিক গঠনসম্পন্ন একটি সুনির্মিত যন্ত্র। অতি সাম্প্রতিককালের আবিষ্কারে পশু ও যন্ত্রের মধ্যকার দৃশ্যমান দূরত্বটি লোপ পেয়েছে। (অর্থাৎ আধুনিক মানুষ পশুপ্রাণীর চলাফেরা, ক্রিয়াকর্মের মধ্যে যন্ত্রের নিয়ম দেখতে পাচ্ছে) অন্যদিকে গ্রিকদের কাছে জড়বস্তুর দৃশ্যমান গতিকে পশুদের চলাফেরার সঙ্গে অঙ্গীভূত করা অধিকতর স্বাভাবিক মনে হতো। তারপরেও একটি শিশু জীবন্ত প্রাণী ও অন্যান্য বস্তুর মধ্যে পার্থক্য করতে পারত এই দেখে যে পশুপ্রাণী নিজে থেকে নড়াচড়া করতে পারে। অনেক গ্রিকের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে অ্যারিস্টটলের বেলায়, এই বৈশিষ্ট্য ছিল পদার্থবিজ্ঞানের একটি সাধারণ তত্ত্বের ভিত। কিন্তু গ্রহ-নক্ষত্রের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি কেমন? পশুদের থেকে তাদের পার্থক্য এই যে তাদের গতি নিয়মিত। কিন্তু এটা হতে পারে কেবল তাদের অধিকতর উৎকর্ষের কারণে। প্রত্যেক গ্রিক দার্শনিক, পরিণত বয়সে পৌঁছে যা-ই ভাবুন না কেন, শৈশবে তারা সূর্য ও চাঁদকে দেবতা মনে করার শিক্ষা পেতেন। অ্যানাক্সাগোরাস সূর্য ও চাঁদকে জীবন্ত মনে করতেন না বলে অধর্মাচরণের দায়ে তার বিচার হয়েছিল। এটা গ্রিস দেশে স্বাভাবিক ছিল যে, একজন দার্শনিক যদি আর মনে করতে না পারেন যে গ্রহ-নক্ষত্রাদি নিজেরা ঐশ্বরিক তবে তিনি অন্তত এটুকু মনে করবেন যে গ্রহ-নক্ষত্রাদি এমন এক ঐশ্বরিক সত্তার ইচ্ছায় পরিচালিত হচ্ছে যে ঐশ্বরিক সত্তার শৃঙ্খলা ও জ্যামিতিক সরলতার প্রতি এক হেলেনিক অনুরাগ আছে। এভাবে, সব গতির চূড়ান্ত উৎস হলো ইচ্ছা। পৃথিবীতে মানুষ ও পশুপ্রাণীর চপল ইচ্ছা, কিন্তু আকাশে সর্বময় স্রষ্টার অপরিবর্তনীয় ইচ্ছা। আমার মনে হয় না অ্যারিস্টটলের সব বক্তব্যের ক্ষেত্রে এ রকম দৃষ্টিভঙ্গি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রযোজ্য। বরং আমার মনে হয়, এ থেকে অ্যারিস্টটলের সমাজের কল্পনাপ্রবণ পটভূমির পরিচয় পাওয়া যায় এবং তদন্ত, পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নেমে অ্যারিস্টটল যে সত্য প্রত্যাশা করেন সে ধরনের জিনিস এতে ফুটে ওঠে।
প্রাথমিক কথাবার্তা হলো, এবার দেখা যাক অ্যারিস্টটল আসলে কী বলছেন। অ্যারিস্টটলের রচনায় পদার্থবিজ্ঞান হলো সেই বিজ্ঞান, গ্রিকরা যাকে বলত Phusis (বা (physis)। শব্দটির ইংরেজি অনুবাদ করা হয়েছে প্রকৃতি (nature)। কিন্তু nature বলতে আমরা যা বুঝি phusis-এর অর্থ হুবহু তা নয়। আমরা এখনো natural science, natural history শব্দগুলো ব্যবহার করি। কিন্তু nature নিজে থেকেই একটি ভীষণ দ্ব্যর্থতাপূর্ণ শব্দ হলেও, phusis দ্বারা যা বোঝাত খুব কদাচিৎ হুবহু তাই বোঝায়। phusis এর সম্পর্ক ছিল বিকাশ-এর সঙ্গে। কেউ বলতে পারেন, একটি ওক বীজের nature হলো একটি ওক গাছে পরিণত হওয়া। তা হলে এক্ষেত্রে বলা যাবে যে, nature হলো অ্যারিস্টটলীয় অর্থে ব্যবহার করা হলো। অ্যারিস্টটল বলছেন, একটি জিনিসের প্রকৃত nature হলো তার লক্ষ্য, অর্থাৎ যে জন্য জিনিসটি অস্তিত্বমান সেই লক্ষ্যটি হলো তার nature। তাহলে দেখা যাচ্ছে শব্দটির একটি উদ্দেশ্যবাদী ব্যঞ্জনার্থ রয়েছে। কিছু কিছু জিনিসের অস্তিত্ব প্রকৃতিগত, কিছু জিনিসের অস্তিত্বের অন্যান্য কারণ থাকে। পশু, উদ্ভিদ এবং সাধারণ বস্তুগুলো (উপাদানগুলো) অস্তিত্বমান হয় প্রকৃতির দ্বারা। তাদের গতির একটি অভ্যন্তরীণ নিয়ম রয়েছে। (গ্রিক যে শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে motion বা movement তার অর্থ Locomotion-এর চেয়ে বিস্ত ততর; সে শব্দটি স্থানান্তরক্ষমতা (locomotion)-এর সঙ্গে গুণের ও আকারের পরিবর্তনকেও নির্দেশ করে। গতিপ্রাপ্ত হবার বা স্থির থাকার একটি উৎস প্রকৃতি বস্তুগুলোর যদি সে ধরনের কোনো অভ্যন্তরীণ নিয়ম থাকে তবে তাদের একটি প্রকৃতি রয়েছে।
প্রকৃতি অনুসারে কথাটি খাটে এই ধরনের বস্তু সম্পর্কে এবং তাদের মৌলিক বৈশিষ্ট্যাবলি সম্পর্কে। (এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই unnatural বা অস্বাভাবিক শব্দটি দ্বারা দোষ বোঝানো হয়।) প্রকৃতি যতটা না বস্তুগত তার চেয়ে বেশি রূপগত। যা সুপ্তরূপে কেবল হাড় ও মাংস তা এখনো তার নিজস্ব প্রকৃতি অর্জন করেনি। সম্পূর্ণতা অর্জনের পর একটি জিনিস কেবল ওই জিনিস থাকে না, তার চেয়ে আরো বেশি কিছু হয়ে ওঠে। এই সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গিটি এসেছে জীববিদ্যা থেকে : একটি ওক ফল একটি ওক বৃক্ষের সম্ভাবনা। প্রকৃতি হলো সেই ধরনের কারণগুলোর অন্তর্গত যেগুলো একটি কিছুর স্বার্থে ক্রিয়া করে। এ থেকে এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে একটি আলোচনা উঠে আসে যে, প্রকৃতি কাজ করে উদ্দেশ্য ছাড়াই, অনিবার্যভাবে।
এই আলোচনার সঙ্গে অ্যারিস্টটলের সবলের টিকে থাকা সম্পর্কিত আলোচনাটির সম্পর্ক রয়েছে অ্যারিস্টটল তা আলোচনা করেছেন এম্পিডকলেস-এর কাছে শেখা পদ্ধতিতে। অ্যারিস্টটল বলছেন, প্রকৃতি উদ্দেশ্যহীন অনিবার্যভাবে কাজ করে-এ কথা সঠিক হতে পারে না, কারণ প্রতিটি ঘটনা ঘটে নির্ধারিত উপায়ে এবং যখন ঘটনার একটি সারি সম্পূর্ণ হয় তখন পূর্ববর্তী সব ধাপ ওই সম্পূর্ণ ঘটনাসারির স্বার্থে কাজ করেছে বলে দেখতে পাওয়া যায়। সেইসব জিনিস হচ্ছে প্রাকৃতিক যেগুলো একটি অভ্যন্তরীণ নিয়ম থেকে উদ্ভূত এক অবিরাম গতির দ্বারা একটি সম্পূর্ণতায় পৌঁছে।
পশু ও উদ্ভিদের বিকাশ ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে প্রকৃতির ধারণাটি সুবিধাজনক হলেও হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতির সম্পূর্ণ ধারণাটি বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে একটি বিরাট প্রতিবন্ধকরূপে দেখা দিয়েছে এবং নীতিশাস্ত্রের ক্ষেত্রে যা কিছু মন্দ কাজ হয়েছে সেসবের একটি উৎস হয়েছে। নীতিশাস্ত্রের ক্ষেত্রে তা এখনো ক্ষতিকর থেকে গেছে।
অ্যারিস্টটল বলছেন, গতি হলো সুপ্তভাবে অস্তিত্বমান কোনো কিছুর পূর্ণায়ন। অন্যান্য দোষ-ত্রুটি ছাড়াও এই দৃষ্টিভঙ্গি সরণের (locomotion) আপেক্ষিকতার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। যখন ক আপেক্ষিকভাবে খ-এর দিকে অগ্রসর হয়, তখন খ-ও আপেক্ষিকভাবে ক-এর দিকে অগ্রসর হয়। (অর্থাৎ ক ও খ-এর মধ্যবর্তী দূরত্ব কমতে থাকে) এ ক্ষেত্রে এ কথা বলার কোনো অর্থ হয় না যে ক ও খ-এর মধ্যে একটি গতিশীল আর অন্যটি স্থির। যখন একটি কুকুর এক টুকরো হাড় লুফে নেয় তখন সাধারণ জ্ঞানে মনে হয় যে কুকুরটি গতিশীল কিন্তু হাড়টি স্থির (না নেওয়া পর্যন্ত), মনে হয় যে গতিটির একটি উদ্দেশ্য আছে, উদ্দেশ্যটি হলো কুকুরটির প্রকৃতির পূর্ণতা ঘটানো। কিন্তু দেখা গেল যে, মৃত বস্তুর ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গি খাটে না, বস্তু ও বল সম্পর্কিত বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যের জন্য লক্ষ্যের কোনো ধারণা কোনো কাজে আসে না। বৈজ্ঞানিক অর্থে কোনো গতিকেই আপেক্ষিক ছাড়া অন্য কিছু মনে করাও যায় না।
লুসিপ্পাস ও ডেমোক্রিটাসের দৃষ্টিভঙ্গির শূন্য অ্যারিস্টটল প্রত্যাখ্যান করেছেন। তারপরে তিনি সময় সম্পর্কে একটি বেশ কৌতূহলপ্রদ আলোচনা শুরু করেন। তিনি বলছেন, মনে করা যেতে পারে যে, সময়ের অস্তিত্ব নেই। কারণ সময় অতীত ও ভবিষ্যৎ নিয়ে গঠিত। আর এ দুয়ের একটির এখন আর অস্তিত্ব নেই এবং অন্যটি এখনো অস্তিত্ব পায়নি। অ্যারিস্টটল এই দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্য বাতিল করেছেন। তিনি বলছেন, সময় হলো একটি গতি, যাতে গণনার অবকাশ আছে (গণনা প্রক্রিয়াকে তিনি কেন অপরিহার্য মনে করছেন তা পরিষ্কার নয়)। তিনি আরো বলছেন, যেহেতু গণনা করার কেউ না থাকলে গণনা করবার কিছু থাকতে পারে না এবং যেহেতু সময় ব্যাপারটা গণনা প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাহলে আমরা সরল মনে প্রশ্ন তুলতে পারি যে আত্মা ছাড়া সময়ের অস্তিত্ব থাকতে পারে কি না। মনে হয়, অ্যারিস্টটল সময়কে অজস্র ঘণ্টা, দিন বা বছর বলে মনে করতেন। তিনি আরো বলছেন, কিছু কিছু জিনিস শাশ্বত। এই অর্থে শাশ্বত যে তারা সময়ের মধ্যে থাকে না। সম্ভবত তিনি সংখ্যার মতো কিছু জিনিসের কথা ভেবে এ কথা বলেছেন। গতি সব সময় ছিল এবং সব সময় তা থাকবে। কেননা গতি ছাড়া সময় হয় না। শুধু প্লেটো ছাড়া সবই একমত যে, সময় কারো দ্বারা সৃষ্ট নয়। এই পর্বে অ্যারিস্টটলের খ্রিস্টান অনুসারীগণ তার সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করতে বাধ্য হয়েছেন, কারণ বাইবেল বলছে যে বিশ্বজগতের একটি শুরু ছিল।
অ্যারিস্টটলের Physics গ্রন্থটি শেষ হয়েছে অনড় চালক-এর পক্ষে একটি যুক্তি প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে। অধিবিদ্যা প্রসঙ্গে আলোচনাকালে আমরা তা নিয়ে আলোচনা করেছি। একজন অনড় চালক রয়েছেন যিনি একটি বৃত্তাকার গতির প্রত্যক্ষ কারণ। বৃত্তাকার গতি হচ্ছে আদি গতি; এটাই একমাত্র গতি যা অবিরাম ও অসীম হতে পারে। আদি চালকের কোনো অংশ বা বিস্তার নেই; আদি চালকের অবস্থান বিশ্বজগতের পরিধি- রেখায়।
এই উপসংহারে পৌঁছার পর আমরা এখন আকাশ সম্পর্কিত আলোচনায় যাব।
অ্যারিস্টটলের On the Heavens সন্দর্ভটিতে একটি প্রীতিকর ও সরল তত্ত্ব উপস্থাপিত হয়েছে। বলা হচ্ছে, চাঁদের নিচে বিরাজমান বস্তুগুলো সৃষ্টি ও বিলয়ের অধীন, আর চাঁদ থেকে উপরের দিকে যা কিছু রয়েছে তার সবকিছুই অসৃষ্ট ও অবিনাশ্য। পৃথিবী গোলাকার এবং তা রয়েছে ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে। চন্দ্ৰতলবর্তী বলয়ে সবকিছু গঠিত ৪টি উপাদান নিয়ে, যথা : মাটি, পানি, বায়ু ও আগুন। তবে একটি পঞ্চম উপাদানও রয়েছে, যা দ্বারা গ্রহ-নক্ষত্রাদি গঠিত। পার্থিব উপাদানগুলোর প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক গতি ঋজুরেখ আর পঞ্চম উপাদানটির গতি বৃত্তাকার। আকাশ পুরোপুরি গোলাকার, আকাশের উপরের অঞ্চলগুলো নিজের অঞ্চলগুলোর চেয়ে অধিকতর ঐশ্বরিক। গ্রহ ও নক্ষত্রগুলো আগুনের তৈরি নয়, বরং ওই পঞ্চম উপাদানে গঠিত। তাদের গতি তাদের সংলগ্ন বলয়ের কারণে। (এ বিবরণের সবটুকু কাব্যিক রূপে পাওয়া যায় দান্তের Paradiso-তে)
পার্থিব উপাদান চারটি শাশ্বত নয়, বরং তাদের একটার সৃষ্টি অন্যটা থেকে। আগুন সম্পূর্ণভাবে হালকা-এই অর্থে যে তার স্বভাবগত গতি ঊর্ধ্বমুখী। মাটি চূড়ান্ত ভাবে ভারী। বায়ু আপেক্ষিকভাবে হালকা, আর পানি আপেক্ষিকভাবে ভারী। এই তত্ত্ব পরবর্তীকালের জন্য অনেক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। ধূমকেতুগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় বলে জানা সম্ভব হয়েছিল এবং সে কারণে ধূমকেতুগুলোকে চন্দ্ৰতলবর্তী বলয়ের বস্তুগুলোর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু ১৭ শতকে আবিষ্কৃত হয়েছে যে ধূমকেতুগুলো সূর্যের চারদিকে তাদের কক্ষপথে আবর্তিত হয়, তারা খুব কদাচিৎ চাঁদের মতো নিকটবর্তী। পার্থিব বস্তুগুলোর প্রাকৃতিক গতি যেহেতু ঋজুরেখ অতএব মনে করা হতো যে, আনুভূমিকভাবে নিক্ষিপ্ত কোনো বস্তু কিছু সময় ধরে আনুভূমিকভাবে অগ্রসর হবে, তারপর হঠাৎ উল্লম্বভাবে পড়তে শুরু করবে। নিক্ষিপ্ত যেকোনো বস্তু উপবৃত্তাকারে অগ্রসর হয়-গ্যালিলিওয়ের এই আবিষ্কারে তার অ্যারিস্টটলবাদী সহকর্মীরা আঘাত পেয়েছিলেন। পৃথিবী যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু নয় এবং তা যে দিনে একবার ঘোরে এবং বছরে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে-এই অভিমত প্রতিষ্ঠার জন্য কোপার্নিকাস, কেপলার ও গ্যালিলিওকে শক্ত লড়াই করতে হয়েছে অ্যারিস্টটল এবং বাইবেলের বিরুদ্ধে।
আরো সাধারণ একটি কথা এই যে, অ্যারিস্টটলের পদার্থবিজ্ঞান নিউটনের প্রথম গতিসূত্রের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। সর্বপ্রথম গ্যালিলিও-এর মুখে উচ্চারিত এই গতিসূত্রটি বলে যে, প্রত্যেক গতিশীল বস্তু, বাইরে থেকে কোনো শক্তি প্রয়োগ করা না হলে, সমবেগে একটি সরলরেখায় চলতে থাকবে। তা হলে, বাইরের কারণ প্রয়োজন গতি ব্যাখ্যা করার জন্যে নয়, বরং গতির পরিবর্তন ব্যাখ্যার জন্যে; হয় গতির বেগ বা তার দিকের পরিবর্তনের জন্যে। বৃত্তাকার গতি (অ্যারিস্টটল যাকে গ্রহ-নক্ষত্রাদির জন্য প্রাকৃতিক গতি মনে করতেন) গতির দিকের একটি অবিরাম পরিবর্তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, আর তাই বৃত্তাকার গতির জন্য বৃত্তের কেন্দ্রাভিমুখী একটি বল প্রয়োজন, যেমনটি ঘটে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্রের ক্ষেত্রে।
আকাশের বস্তুগুলো শাশ্বত এবং অনশ্বর-এই দৃষ্টিভঙ্গি শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয়েছে। সূর্য ও তারকাদের জীবন দীর্ঘ কিন্তু তাদের পরমায়ু নেই। তাদের জন্ম হয়েছে একটি নীহারিকা থেকে এবং পরিণতিতে তারা হয় বিস্ফোরিত হবে নয় ঠাণ্ডায় মরে যাবে। দৃশ্যমান জগতের কোনো কিছুই পরিবর্তন ও বিনাশের হাত থেকে রেহাই পাবে না। অ্যারিস্টটলের বিশ্বাস ঠিক এর উল্টো। এ হচ্ছে চন্দ্র-সূর্য ও গ্রহ-নক্ষত্রাদির পৌত্তলিক উপাসনার একটি ফসল, যদিও মধ্যযুগীয় খ্রিস্টানরা তা গ্রহণ করেছিলেন।