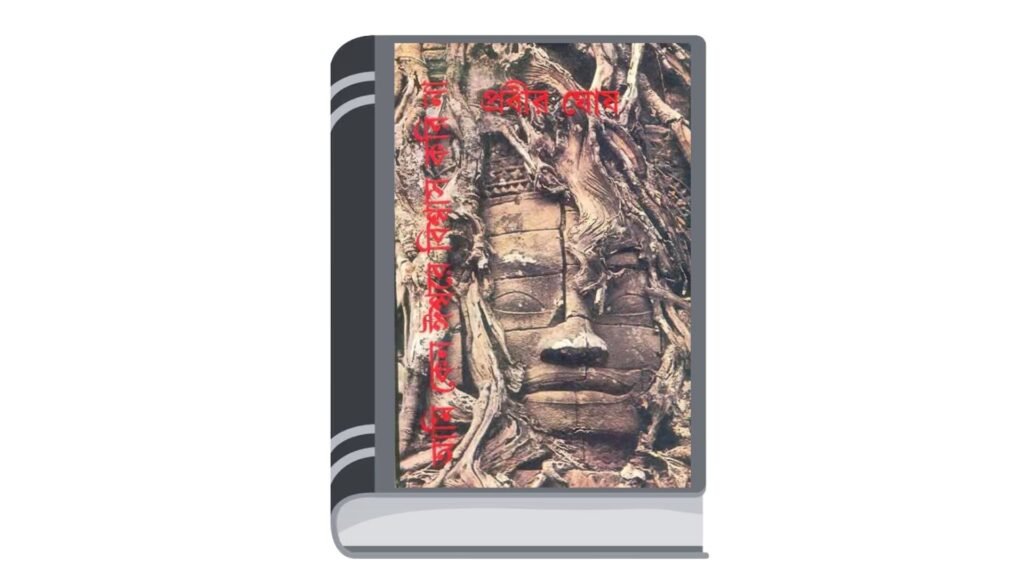৮. নাস্তিকতা-মানবতা-যুক্তিবাদ ও প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা
অধ্যায়: আট
ঈশ্বর বিশ্বাস: নাস্তিকতা-মানবতা-যুক্তিবাদ ও প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা
‘নাস্তিকতা’ ও ‘মানবতা’
ধর্ম যাদের ‘মানবতা’, তাদের নাস্তিক বলে চিহ্নিত করলে একটা বড় রকমের ভুল করা হবে। এই বক্তব্যের যৌক্তিকতা বোঝাতে যা প্রয়োজন তা হল, ‘নাস্তিকতাবাদ’ ও ‘মানবতাবাদ’ নিয়ে কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা।
নাস্তিকতাবাদ’ ও ‘মানবতাবাদ’ শব্দ দুটি সমার্থক তো নয়ই, বরং সুস্পষ্ট একটা পার্থক্য রয়েছে। ‘নাস্তিকতাবাদ’-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ ‘Atheism’। ‘Atheism’ শব্দের আভিধানিক অর্থ ‘নিরীশ্বরবাদ’। অর্থাৎ ‘ঈশ্বরের অস্তিত্বকে মানা মতবাদ’।
নাস্তিক’ শব্দের বাংলা আভিধানিক অর্থ অবশ্য কিঞ্চিৎ বিস্তৃত। ‘সাহিত্য সংসদ’ প্রকাশিত ‘বাঙ্গালা ভাষার অভিধান’ বলছে, ১) যে বেদ মানে না; যে বেদকে আপ্তবাক্য বলিয়া স্বীকার করে না; ২) যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, বেদ ও পরকাল স্বীকার করে না; ৩) দেশাচার যে মানে না।
‘সাহিত্য সংসদ’ প্রকাশিত অভিধানের লেখক জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ‘নাস্তিক’ শব্দের অর্থ হিসেবে যখন বলেন, “যে বেদ মানে না; যে বেদকে আপ্তবাক্য বলিয়া স্বীকার করে না তখন সেই বলার মধ্যে প্রকাশিত হয় হিন্দু ধর্ম-শাস্ত্রের দেওয়া ‘নাস্তিক’ শব্দের ব্যাখ্যা।
হিন্দু ধর্মের দেওয়া ‘নাস্তিক’ শব্দের সংজ্ঞাটি আমরা প্রথমেই বাতিল করছি। কারণ, এই সংজ্ঞাকে মেনে নিলে হিন্দু ধর্ম ছাড়া যে কোনও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাসীকেও ‘নাস্তিক’ বলে চিহ্নিত করতে হয়। অথচ বাস্তবে অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মাবলম্বীরা কেউই ‘atheist’-এর দেওয়া সংজ্ঞায় পড়েন না।
বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম যদিও ‘নিরীশ্বরবাদী’ অর্থাৎ ঈশ্বর বা পরমাত্মায় বিশ্বাসী নয়, তবু এই দুই ধর্মকে ‘নাস্তিক’ বলে চিহ্নিত করলে ভুল করা হবে। কারণ, এই দুই ধর্মই আত্মায় বিশ্বাসী এবং হিন্দু ধর্মের প্রভাবে, জন্মান্তরে বিশ্বাসও প্রবল। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে বিশ্বাসীরাও তাঁদের ধর্মের বিধানকে তাঁদের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আচার বা দেশাচার বলে মান্য করেন।
সাংখ্য ও ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের অবস্থা বেশ গোলমেলে। চিন্তায় কিছুটা বস্তুবাদের ছোঁয়া থাকলেও আত্ম-অদৃষ্ট-কর্মফল-পুনর্জন্ম-চতুর্বর্ণ ইত্যাদি বিষয়কে মেনে নিয়ে স্ববিরোধিতার আবর্তে পাক খাচ্ছে।
‘নাস্তিকতাবাদ’ শব্দটি আমরা কখনও কখনও ‘যুক্তিবাদ’ বা ‘বস্তুবাদ’ শব্দের পরিবর্ত হিসেবে ব্যবহার করি। যেমন—বিজ্ঞান যতই এগুচ্ছে, ততই নাস্তিকতার পথে হাঁটছে’। বাক্যটিতে ‘নাস্তিকতা’ শব্দটি ব্যবহার না করে ‘যুক্তিবাদ’ বা ‘বস্তুবাদ’ শব্দটি নিয়ে এলে বাক্যটি আরও সুবিন্যস্ত হতো। কারণ, সাধারণভাবে, মূলগতভাবে ‘নাস্তিকতাবাদ’ বলতে বুঝি সেই মতবাদ, যা আত্মা-পরমাত্মার অস্তিত্বকে বিশ্বাস করে না, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিধানকে মান্য করে না। মানবতাবাদ’-এর সঙ্গে ‘নাস্তিকতাবাদ’-এর মিল এইখানে যে, মানবতাবাদও আত্মা-পরমাত্মার অস্তিত্বকে এবং প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিধানকে মান্য করে না। অমিলও প্রচুর।
নাস্তিকতাবাদে যুক্তিহীন অধ্যাত্মবাদী চিন্তাকে বাতিল করার ঝাঁজ যতখানি উপস্থিত, ততখানিই অনুপস্থিত ভবিষ্যম্মুখী মানবতাবাদী সমাজ সচেতনতা বোধ। বহুক্ষেত্রেই নাস্তিকদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী, উন্নাসিকতা, আর্থ-সামাজিক ও সমাজ-সাংস্কৃতিক বিষয়ে স্বচ্ছ ও সুসংবদ্ধ চিন্তার অভাব। যাই হোক, আমরা নিশ্চয়ই বলতে পারি, শুধুমাত্র আত্মা-পরমাত্মার অস্তিত্বকে এবং প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিধানকে অস্বীকার করাই সাম্যের সুন্দর সমাজ গড়ার পক্ষে অবশ্যই যথেষ্ট নয়। কারণ, ‘নাস্তিকতাবাদ’ শব্দটি সাধারণত যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাতে অনুপস্থিত থাকে মানবিক মূল্যবোধের নিরিখে নিজের জীবনচর্যাকে পরিচালিত করে সমাজ-বিকাশকে প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা।
O
নাস্তিকতাবাদে যুক্তিহীন অধ্যাত্মবাদী চিন্তাকে বাতিল করার ঝাঁজ যতখানি উপস্থিত, ততখানিই অনুপস্থিত ভবিষ্যৎমুখী মানবতাবাদী সমাজ সচেতনতা বোধ।
O
এই প্রসঙ্গের সূত্র ধরে এটুকু মনে করিয়ে দিতে চাই, ভারতবর্ষের নাস্তিক্যবাদ দর্শনের এক বিরাট অংশ জুড়ে থাকা চার্বাক দর্শনে আর্থসামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটিয়ে সাম্যের সমাজ গড়ার কোনও চিন্তা ছিল না। তাই চার্বাক দর্শন গণশক্তি নির্ভর ও সক্রিয় রূপ ধারণ করতে পারেনি। এ’দেশের প্রাচীন ধর্মসূত্রগুলো যেমন পরিপূর্ণভাবে রাজতন্ত্রের সমর্থক ছিল, চার্বাকবাদীরাও ছিল তেমনই সেই সময়কার রাজতন্ত্রকেন্দ্রীক শোষণ কাঠামোর সমর্থক। তাঁরাও মনে করতেন, “লোকসিদ্ধো ভবেদ্রাজা পরেশো নাপরঃ স্মৃতঃ”। অর্থাৎ রাজার উপরে কোনও পরমেশ্বর নেই।
O
এদেশের প্রাচীন ধর্মসূত্রগুলো যেমন পরিপূর্ণভাবে রাজতন্ত্রের সমর্থক ছিল, চার্বাকবাদীরাও ছিল তেমনই সেই সময়কার রাজতন্ত্রকেন্দ্রীক শোষণ কাঠামোর সমর্থক।
O
একজন মানবতাবাদীর মধ্যে দার্শনিক আত্মোপলব্ধি রয়েছে। সে যুক্তির পথ ধরে সব কিছুকে বিচার করে। তার সংঘর্ষের মধ্যেও থাকে সুন্দর সমাজ বিকাশের প্রেরণা; মানুষকে মানুষ করে তোলার প্রেরণা। অর্থাৎ, মানবতাবাদ নাস্তিকতাবাদের সঙ্গে বাড়তি কিছু।
নিছক নাস্তিকতাবাদ যেহেতু এক ধরনের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী, সেহেতু এই মতবাদ কখনই মানুষের ‘সুগুণ’ বা ‘সুবৈশিষ্ট্য’-এর পরিচয় বহন করে না। শুধুমাত্র ‘নাস্তিকতাবাদ’ বা ‘নিরীশ্বরবাদিতা’ ও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে অবিশ্বাস মানুষের আদর্শ আচরণ বিধি বা আদর্শ জীবন যাপন পদ্ধতি হয়ে উঠতে পারে না। এবং শেষ পর্যন্ত ‘নাস্তিকতাবাদ’ মানুষের মানুষ হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় গুণ হয়ে ওঠে না। অর্থাৎ, শেষতক ‘নাস্তিকতাবাদ’ মানুষের ‘ধর্ম’ হয়ে উঠতে পারে না।
O
শুধুমাত্র ‘নাস্তিকতাবাদ’ বা ‘নিরীশ্বরবাদিতা’ ও ‘প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে অবিশ্বাস’ মানুষের আদর্শ অচিরণ বিধি বা আদর্শ জীবন যাপন পদ্ধতি হয়ে উঠতে পারে না।
O প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, আপনারাই পারেন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম, রাষ্ট্রশক্তি ও প্রচারমাধ্যমগুলোর পরিকল্পিত এক ষড়যন্ত্রকে বানচাল করে দিতে। জনতার মগজ ধোলাইয়ের জন্য খরচ করা বিপূল শ্রম ও ব্যয়কে ফালতু করে দিতে। আপনারাই পারেন মানুষের ধর্মকে মানুষের কাছে শুভকর, ইতিবাচক ও মানবিক করে তুলতে। প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, আজ থেকে চিন্তায়, কথায়, লেখায় ‘ধর্ম’-এর সংজ্ঞা নিরূপণ করুন ‘বৈশিষ্ট্য’ বা ‘গুণ’-এর নিরিখে। আর তবেই, এবং শুধুমাত্র তবেই, মানুষের একমাত্র ‘ধর্ম’ হয়ে উঠবে ‘মনুষ্যত্ব’ বা ‘মানবতা।
‘ধর্ম’ যেখানে ‘গুণ’, মূল্যবোধ যেখানে ‘মানবতা’
‘ধর্ম যেখানে অলীক চিন্তায় নুব্জ নয়, বেঁধে দেওয়া আচরণবিধিতে বন্দি নয়, স্থবির অনড় মূল্যবোধের শৃঙ্খলে শঙ্খলিত নয়, ধর্ম যেখানে ‘বৈশিষ্ট্য’ বা ‘গুণ’, ‘ধর্ম’ যেখানে মনুষত্ব’ বা ‘মানবতা’ সেখানেই ‘ধর্ম’ শব্দটি অর্থবহ ও সার্থক হয়ে ওঠে।
যুক্তির পথ হাঁটা মানবতাবাদী মানুষের ‘মূল্যবোধ’ কোনও ছক বাঁধা বিধান নির্ভর হতে পারে না। সময় ও সমাজ অনুসারে মূল্যবোধ পাল্টায়। মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি বা পশ্চাৎমুখিতার সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবোধও পাল্টে যায়।
প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিধান মেনে যিনি জীবনকে চালিত করেন, তিনি ধার্মিক। ‘ধার্মিক মানুষ’ সমাজ সচেতন মানুষদের চোখে আদর্শ মানুষ হবেন না, এটাই স্বাভাবিক। তার মানে এই নয় যে, ‘নাস্তিক মানুষ’ অর্থাৎ ঈশ্বর, আত্মা ও ধর্মীয় বিধানে অবিশ্বাসী মানুষ মানেই আদর্শ মানুষ (অবশ্য হিন্দু ধর্মের বিধান-দাতা মনুর কথা মত—যে ‘শ্রুতি’ ও ‘স্মৃতি’র একটিকেও অবজ্ঞা করে, তাকে বেদবিরোধী ও নাস্তিক বলে গণ্য করতে হবে। ফলে হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস মতে “হিন্দু ভিন্ন অন্যানা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাসী মাত্রেই ‘নাস্তিক’)।
‘আদর্শ মানুষ’ হতে গেলে মানুষটিকে যেমন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে, তেমনই ‘মানবিক মূল্যবোধ’ দ্বারা নিজের আচরণবিধিকে পরিচালিত করতে হবে।
O
‘আদর্শ মানুষ’ হতে গেলে মানুষটিকে যেমন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম থেকে বিভিন্ন হতে হবে, তেমনই ‘মানবিক মূল্যবোধ’ দ্বারা নিজের আচরণবিধিকে পরিচালিত করতে হবে।
O
মূল্যবোধ’ শব্দটি বাপকভাবে ব্যবহৃত হলেও শব্দটির অর্থ বা সংজ্ঞা অনেকের কাছেই অধরা। সত্যি বলতে কি, প্রায়শই শব্দটি ব্যবহারকারিদের কাছেও অধরা। তাই মূল্যবোধ নিয়ে আলোচনা এক্ষেত্রে অতি প্রাসঙ্গিক।
‘মূল্যবোধ’ শব্দটি ‘মূল্য’ এবং ‘বোধ’ শব্দদুটির সমষ্টি। ‘মূল্য’ বলতে আমরা সাধারণভাবে বুঝি কোনও কিছুর সঙ্গে মুদ্রার বিনিময় হার। কিন্তু আমরা যদি বলি—’পথের পাঁচালী’ বিদেশ থেকে সম্মান আনার আগে আমরা সত্যজিৎ রায়ের প্রতিভার সঠিক মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছিলাম, এই বাক্যটির ক্ষেত্রে মূল্য শব্দটি মুদ্রার বিনিময় হার হিসেবে প্রয়োগ করা হয়নি। এখানে মূল্যায়ন শব্দটি ‘যোগ্যতা নিরূপণ’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
‘বোধ’ শব্দের অর্থ “জ্ঞান’, ‘বুদ্ধি’, ‘চৈতন্য’, ‘বোঝ।’ অর্থাৎ কোনও ঘটনা মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে-তাই হল সে সম্পর্কে আমাদের বোধ।
‘মূল্যবোধ’ শব্দটির একটা গ্রহণযোগ্য অর্থ আমরা পেলাম-‘যোগ্যতা বোঝা’ বা ‘যোগ্যতা নিরূপণ’-এর ক্ষমতা এবং প্রবণতা। Value-র বাংলা অর্থ ‘যোগ্যতা’। ‘Sense of value’-র বাংলা হিসেবেই আমরা মূল্যবোধ শব্দটি ব্যবহার করি, ‘Price’-এর বাংলা অর্থ হিসেবে নয়। এই ‘মূল্যবোধ’ শব্দটির সাহায্যে আমরা কোনও কিছুর ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত ইত্যাদির যোগ্যতা পরিমাপ করি।
এই ‘বোধ’ বা ‘যোগ্যতা’ বোঝার ক্ষমতা সবার সমান নয়। তথাকথিত অলৌকিক রহস্য ভেদের ক্ষেত্রে আমার যা বোধশক্তি তা একজন জারোয়ার চেয়ে যতগুণ বেশি, তারচেয়েও বোধহয় বেশিগুণ বেশি আমার ফুটবল বোধশক্তির তুলনায় পেলে বা মারাদোনার ফুটবল বোধশক্তি।
‘মূল্যবোেধ’ আপেক্ষিক। মৃলোর যে পরিমাপ আপনি করছেন, অর্থাৎ যোগ্যতা নিরূপণ করছেন, তা অন্যের কাছে খারাপ মনে হতে পারে, আবার ভালও মনে হতে পারে। আপনার কাছে যা আদর্শ, অন্যের কাছে তা অনাদর্শও হতে পারে। সময় ও সমাজ অনুসারে মূল্যবোেধ পাল্টায়। আবার একই দেশের মানুষদের অগ্রসর অংশেৱা যে মূল্যবোধে বিশ্বাস করে, সেই মূল্যবোধ পিছিয়ে থাকা মানুষদের চোখে অবক্ষয় মনে হতেই পারে। এক সময় সমাজের এক বৃহৎ অংশ মনে করত, স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাওয়াটাই নারী জীবনের চরম মূল্যবোধ। এক সময় নারী-শিক্ষা, বিধবা-বিবাহ ইত্যাদি অনগ্রসর ও রক্ষণশীলদের চোখে সমাজের অবক্ষয় বলেই ঘোষিত হয়েছে। রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা রোধে আন্দোলন করেছিলেন, বিদ্যাসাগর নারী-শিক্ষা ও বিধবা বিবাহের পক্ষে আন্দোলন করেছিলেন। রামমোহন রায় ও বিদ্যাসাগরের এই আন্দোলন অনেকের চোখেই খারাপ ঠেকেছে। তাদের মনে হয়েছে, এই আন্দোলন সমাজের অবক্ষয় ঘটাবে। আবার রামমোহন, বিদ্যাসাগরের চিন্তায় প্রভাবিত মানুষদের চোখে এই আন্দোলন মোটেই অবক্ষয় ছিল না, ছিল শ্রেয় মূল্যবোধ, যা সমাজ পোষণ করছে না। মূল্যবোধ আপেক্ষিক বলেই বিধবা বিবাহ, নারী শিক্ষা কারও চোখে ভাল, কারও চোখে খারাপ বলে মনে হয়েছে।
O
একই দেশের মানুষদের অগ্রসর অংশেরা যে মূল্যবোধে বিশ্বাস করে, সেই মূলবোধ পিছিয়ে থাকা মানুষদের চোখে অবক্ষয় মনে হতেই পারে। এক সময় সমাজের এক বৃহৎ অংশ মনে করত, স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাওয়াটাই নারী জীবনের চরম মূল্যবোধ।
O
‘মূল্যবোধ’ বিষয়টিকে এবার আমরা মনস্তত্ব ও সমাজতত্বের দিক থেকে ভাববার চেষ্টা করি আসুন। মনস্তত্ব ব্যক্তি ভাবনাকে ব্যাখ্যা করে, সমাজতত্ব ব্যাখ্যা করে যৌথ ভাবনাকে, গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবনাকে। আপাতভাবে মনে হতে পারে, ব্যক্তির সমষ্টিকে নিয়েই যখন সমাজ, তখন অনেক ব্যক্তি-ভাবনার বাখ্যা থেকেই তো সমষ্টির ভাবনার হদিশ মেলা উচিত অথবা গোষ্ঠীর ভাবনা ধরে আমরা পৌছতে পারি ব্যক্তি ভাবনায়। আসলে বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যাপারটা তেমন অতি সরলীকৃত নয় যে, সবসময় ব্যক্তি ভাবনা থেকে গোষ্ঠী ভাবনায় অথবা গোষ্ঠী ভাবনা থেকে ব্যক্তি ভাবনায় পৌঁছে যাওয়া যায় সহজ সরল নিয়মের সহায়তায়। অফিস টাইমের ট্রেনের একটি লেডিজ কামরায় যদি সমীক্ষা চালান, দেখতে পাবেন, এঁদের প্রায় প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে সুকুমারবৃত্তি, সুন্দরের প্রতি ভালোবাসা, নাচ, গান, সাহিত্য, নাটক, সিনেমার প্রতি টনে টান। এঁরাও ব্যক্তিজীবনে কারও না কারও স্নেহময়ী জননী, ভগ্নী, কারও প্রেমময়ী প্রেমিকা, কারও স্ত্রী, কারও বা কন্যা। ব্যক্তি ভাবনার এমন মহিলাদেরই সমষ্টিগত অন্য এক চেহারার পরিচয় পেয়েছি মাঝে-মধ্যে। কখনও কখনও খবরের কাগজের খবর হয়েছে লেডিজ কম্পার্টমেণ্টে হঠাৎ উঠে পড়া কোনও পুরুষকে মহিলা গোষ্ঠীর তীব্র অপমান ও শারীরিক লাঞ্ছনা থেকে বাঁচতে লাফিয়ে পড়ে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে। কম্পার্টমেণ্টে একটি পুরুষকে একা পেতেই সম্মিলিত মহিলাদের যে নিষ্ঠুরতা প্রকট হয়েছে, তার হদিশ পেতে ব্যক্তি ভাবনা ছেড়ে যৌথ ভাবনাকে ব্যাখা করতে হবে। ইট দিয়ে বাড়ি তৈরি হলেও বাড়ি যেমন শুধুমাত্র ইটের পর ইট সাজানোর ব্যাপার নয়, তেমনই ব্যক্তি নিয়ে সমাজ হলেও, সমাজ শুধু ব্যক্তির সমষ্টি নয়, বাড়তি কিছু। তাই শুধুমাত্র মনস্তত্বের সাহায্যে সমাজ জীবনের ভাবনা বা সমাজ জীবনের ধারাকে ধরা নাও যেতে পারে।
অনেক সময় এমন হয়েছে, ব্যক্তিগত মূল্যবোধ শেষ অবধি সামাজিক মূল্যবোধে রূপান্তরিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার চিন্তা ভাবনার দ্বারা বহুকে প্রভাবিত করেছে, বহু থেকে বহুতরতে ছড়িয়ে পড়েছে সেই চিন্তার রেশ। এই ভাবনা এক থেকে বহুতে ছড়িয়ে পড়ার মধ্যে, গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবনাতে রূপ পাওয়ার মধ্যে যে প্রক্রিয়া, পদ্ধতি বা তত্ব রয়েছে—সেও সমাজতত্ত্ব।
O
অনেক সময় এমন হয়েছে, ব্যক্তিগত মূল্যবোধ শেষ অবধি সামাজিক মূল্যবোধে রূপান্তরিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার চিন্তা ভাবনার দ্বারা বহুকে প্রভাবিত করেছে, বহু থেকে বহুতরতে ছড়িয়ে পড়েছে সেই চিন্তার রেশ।
O
‘মূল্যবোধ’ বিষয়টি মনস্তত্বের দিক থেকে একটু ভাববার চেষ্টা করা যাক। ব্যক্তি মানুষের মূল্যবোধ বা নীতিবোধের প্রকাশ ও বিকাশ তার সামাজিক পরিবেশের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। পরিবেশগতভাবে কিছু মানুষের মনে হতেই পারে—ঈশ্বরে অবিশ্বাস নীতিহীনতারই পরিচয়, যুক্তিহীনতারই পরিচয়, মূল্যবোধের অবক্ষয়েরই পরিচয়। আবার এই সামাজিক পরিবেশের প্রভাবেই কেউ কেউ মনে করতে পারেন—যুক্তিহীন ঈশ্বর বিশ্বাস, অদৃষ্ট-বিশ্বাস, নীতিহীন অন্ধ কুসংস্কার বই কিছুই নয়। বিপরীত মানসিকতার এই দুই শ্রেণীর মানুষই কিন্তু পরিবেশগত ভাবেই প্রভাবিত হয়েছেন। এই প্রভাব ফেলার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারে, পরিচিত মানুষ, আত্মীয়, বন্ধু, শিক্ষক, প্রচারমাধ্যম, সাহিত্য, নাটক, চলচ্চিত্র, দূরদর্শন, আলোচনা সভা, বই-পত্তর, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি অনেক কিছুই, বা এরই কোনও একটি যা মনকে বিপুলভাবে নাড়া দিয়েছে।
এমন বক্তব্য পেশ করার পর কেউ প্রশ্ন করে বসতে পারেন, আমাদের মানসিক বৈশিষ্ট্য যদি পুরোপুরি জিন বা বংশগতি প্রভাবিত না হয়ে পরিবেশ দ্বারাই বেশি প্রভাবিত হয়, অর্থাৎ আমাদের মানসিক বৃত্তির উপর বংশগতির চেয়ে পরিবেশই যদি বেশি প্রভাবশালী হয়, তবে অনুকূল পরিবেশের মধ্যে রেখে পশুদের মধ্যেও তো মানবিক-গুণ বা মানবিক-বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটানো সম্ভব—এমন তত্বকেও মেনে নিতে হয়।
O
আমরা যে দু’পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াই, হাঁটি, পানীয় পশুর মতন জিব দিয়ে চেটে গ্রহণ না করে পান করি, কথা বলে মনের ভাবপ্রকাশ করি—এসবের কোনওটাই জন্মগত নয়। এইসব অতি সাধারণ মানব-ধর্মগুলোও আমরা শিখেছি, অনুশীলন দ্বারা অর্জন করেছি। শিখিয়েছে আমাদের আশেপাশের মানুষগুলো
O
দু-এককথায় উত্তরটা এই—মানবশিশু প্রজাতিসুলভ জিনের প্রভাবে মানবধর্ম বিকশিত হবার পরিপূর্ণ সম্ভাবনা (potentialities) নিয়ে অবশ্যই জন্মায়। কিন্তু সম্ভাবনাকে বাস্তব রূপ দেয় মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-বন্ধু, শিক্ষক, অধ্যাপক, সহপাঠী, খেলার সঙ্গী, পরিচিত ও আশেপাশের মানুষেরা অর্থাৎ সামাজিক পরিবেশ। আমরা যে দু’পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াই, হাঁটি, পানীয় পশুর মতন জিব দিয়ে চেটে গ্রহণ না করে পান করি, কথা বলে মনেরভাব প্রকাশ করি—এসবের কোনওটাই জন্মগত নয়। এইসব অতি সাধারণ মানব-ধর্মগুলোও আমরা শিখেছি, অনুশীলন দ্বারা অর্জন করেছি। শিখিয়েছে আমাদের আশেপাশের মানুষগুলো, অর্থাৎ আমাদের সামাজিক পরিবেশ। এই মানবশিশুই কোনও কারণে মানুষের পরিবর্তে পশু সমাজের পরিবেশে বেড়ে উঠতে থাকলে তার আচরণে, হাঁটা-চলা, খাদ্যাভ্যাসে, পানীয় গ্রহণের কায়দায়, ভাব বিনিময়ের পদ্ধতিতে পশু সমাজের প্রভাবই প্রতিফলিত হবে। কিন্তু একটি বনমানুষ বা শিম্পাঞ্জিকে শিশুকাল থেকে আমাদের সামাজিক পরিবেশে মানুষ করলেও এবং আমাদের পরিবারের শিশুর মত তাকেও লেখাপড়া শেখাবার সর্বাত্মক চেষ্টা চালালেও তাকে আমাদের সমাজের স্বাভাবিক শিশুদের বিদো, বুদ্ধি, মেধার অধিকারী করতে পারব না; কারণ এই বনমানুষ বা শিম্পাঞ্জির ভিতর বংশগতির ধারায় বংশানুক্রমিক মানবিক গুণ না থাকায় তা অনুকূল পরিবেশ পেলেও বিকশিত হওয়া কোনওভাবেই সম্ভব নয়। অর্থাৎ মানব গুণ বিকাশে জিন ও পরিবেশ দুয়েরই প্রভাব বিদ্যমান।
আবার একই পরিবেশের মধ্যে বেড়ে ওঠা বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার পরিচয়ও আমরা পাই বই কি। কেন এমনটা হয়? এই প্রসঙ্গে মনস্তত্ব নিয়ে আসবে বিভিন্ন ব্যক্তি মানুষের বিভিন্ন প্রবণতার কথা। যমজ হওয়ার সুবাদে একই ধরণের গাত্র-বর্ণ, একই ধরনের দেহ-গঠন এবং একই ধরনের মুখাকৃতি হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেক ব্যক্তিমানুষ স্বতন্ত্র—’ইণ্ডিভিজুয়াল’। প্রত্যেক মানুষের মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের গতিময়তা, উত্তেজনা-নিস্তেজনা, আবেগপ্রবণতা বা সংবেদনশীলতা ইত্যাদি ধর্মগুলো ভিন্নতর। তাই একই সামাজিক পরিবেশের প্রভাবে বেড়ে ওঠার দরুণ সাধারণভাবে ও সামগ্রিকভাবে সেই পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হলেও সেই প্রভাবেরও নানা তারতম্য ঘটে, রকমফের ঘটে। এমন কি ভিন্নতর, নতুন চিন্তা-ভাবনার উন্মেষও দেখা যায়। অনেক সময়ই দেখা যায় সমাজতত্ত্ব ও মনস্তত্ব উভয় উভয়ের সঙ্গে একটা বিরোধের ভাব পোষণ করে থাকে, সমাজতত্ত্ব যেন একটা ধারণা উপর থেকে চাপিয়ে দিচ্ছে। ব্যক্তির উপর বহুর চিন্তা বা শাসকশ্রেণীর চিন্তা চাপানোর মধ্যে অনেক সময় দেখা দেয় বিরোধ।
O
সমাজসেবার মাধ্যমে শোষণ-মুক্তি ঘটেছে, এমন দৃষ্টান্ত আজ পর্যন্ত কোনও ঐতিহাসিকের জ্ঞান ভাণ্ডাবে নেই। হাজারটা রামকৃষ্ণ মিশন, হাজারটা ভারত সেবাশ্রম সংঘ, হাজার মাদার টেরিজার সাধ্য নেই ভারতের শোষিত-জনতার শোষণমুক্তি ঘটানোর।
O
যে সমাজে শোষণ আছে, সে সমাজে শোষিত থাকবেই। থাকবে শোষক। শোষকরা তাদের প্রতিনিধিদের দ্বারাই চালিয়ে থাকে শাসন। নির্বাচন নির্ভর গণতন্ত্রে বাক্সে জেতার মত ভোট ফেলতে ‘বুথ জ্যাম’, ‘রিগিং’, মস্তানবাহিনী, প্রচার, এজেণ্ট নিয়োগ ইত্যাদি ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই এগোতে হয়—যা বিপুল ব্যয়সাধ্য, এবং যে ব্যয়ভারের প্রায় পুরোটাই জোগায় শোশাষকশ্রেণী। তার ফলশ্রুতিতে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শাসকশ্রেণী শোষকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনে বহু নীতিবোধ বা মূল্যবোধ সমাজের উপর চাপিয়ে দেয় এই নীতিবোধ বা মূল্যবোধ ব্যাপক প্রচারের ফলে, ব্যাপক মগজ ধোলাইয়ের ফলে বহুর কাছেই গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে। বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তা, সমাজ সচেতনতা, রাজনৈতিক বিশ্বাস থেকে অথবা নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান ও বিজ্ঞান পড়ার ফলে, কিংবা সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়ার ফলে আমরা যদি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোই-এক: দেশপ্রেম মানে দেশের মাটির প্রতি প্রেম নয়, দেশের সংখ্যাগুরু মানুষের প্রতি প্রেম। দুই: সমাজসেবার মাধ্যমে শোষণ-মুক্তি ঘটেছে, এমন দৃষ্টান্ত আজ পর্যন্ত কোনও ঐতিহাসিকের জ্ঞান ভাণ্ডাবে নেই। হাজারটা রামকৃষ্ণ মিশন, হাজারটা ভারত সেবাশ্রম সংঘ, হাজার মাদার টেরিজার সাধ্য নেই ভারতের শোষিত-জনতার শোষণমুক্তি ঘটানোর। তিন: ঈশ্বর, ভূত, কর্মফল, অদৃষ্টবাদ ও অলৌকিকত্বের বাস্তব কোনও অস্তিত্ব নেই। শোষক ও শাসকশ্রেণী শোষণকে কায়েম রাখতেই শোষিতদের মধ্যে এই ভ্রান্ত চিন্তাগুলোর প্রসারকামী। চার: দাম্পত্যজীবন গড়ে তোলার প্রথম শর্ত হওয়া উচিত বন্ধুত্ব,যৌন স্বত্বাধিকার নয়—ইত্যাদি আরও বহুতর মূল্যবোধ সম্পর্কিত ধারণায়, তবে এই পরিবর্তনটা হবে অবশ্যই কাম্য। পূর্বতন পুরুষদের কাছে, সংখ্যাগুরু মানুষদের কাছে, পশ্চাৎবর্তী মানুষদের কাছে, মগজ ধোলাইয়ের শিকার মানুষদের কাছে আমাদের অগ্রবর্তী চিন্তার ফসল হিসেবে গড়ে ওঠা মূল্যবোধকে ‘মূল্যবোধের অবক্ষয়’ মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে যুক্তিবাদী, প্রগতিবাদী, সুস্থচেতনার মুক্তিকামী মানুষদের কাছে এই যুগোচিত পরিবর্তিত চিন্তা মূল্যবোধের উত্তরণ, এই মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠার অর্থ অবৈজ্ঞানিক মূল্যবোধের ক্ষয়। মূল্যবোধের পরিবর্তন মানেই ‘অবক্ষয়’ অবশ্যই নয়। শাসকশ্রেণীর চাপিয়ে দেওয়া নীতির ব্যক্তিগতভাবে প্রতিবাদ করার অধিকার আপনার, আমার সবার সব সময়ই থেকে যাবে। এই প্রতিবাদকেই আপনি, আমি সক্রিয় চেষ্টার ফলে যৌথ চেহারা দিতে পারি। কাজেই সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিগত মূলাবোধের সম্পর্ক একটা সচল সম্পর্ক। এমন হতেই পারে—আপনার, আমার ব্যক্তিগত মূল্যবোধ শেষ পর্যন্ত জনসমর্থন পেয়ে সামাজিক মূল্যবোধ হয়ে উঠতে পারে। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিগত মূল্যবোধের সম্পর্ক একই সঙ্গে বিরোধ এবং সংহতির।
O
সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিগত মূলাবোধের সম্পর্ক একটা সচল সম্পর্ক। এমন হতেই পারে—আপনার, আমার ব্যক্তিগত মূল্যবোধ শেষ পর্যন্ত জনসমর্থন পেয়ে সামাজিক মূল্যবোধ হয়ে উঠতে পারে।
O
‘মানবিক মূল্যবোধ’ বা নিপীড়িতের স্বার্থে, সাম্যের স্বার্থে, প্রগতির স্বার্থে, যুক্তির পথ ধরে উঠে আসা মূলবোধ-এর সঙ্গে ধর্মের বেঁধে দেওয়া মূল্যবোধের বিপরীতমুখিতা বা বিরোধ একথাই প্রমাণ করে-ধর্ম যাঁদের মানবতা, তাঁদের যুক্তির বিচারে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের নির্দেশ মানা মূলগতভাবেই মানবিক নয়, বরং বহুক্ষেত্রেই মানবতা বিরোধী এবং আদর্শ বিরোধী জীবন যাপন পদ্ধতি।
‘যুক্তিবাদ’-এর বিরুদ্ধে ‘জ্ঞানবাবা’দের ষড়যন্ত্র বুর্জোয়া মতাদর্শকে টিকিয়ে রাখতেই।
গভীর বিস্ময় ও শঙ্কার সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করছি, এক সময়ের টুকটুকে লাল বিপ্লবীদের কেউ কেউ এক নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ। এঁদের কেউ কেউ এখন ‘জ্ঞানবাবা’। যুক্তিবাদী আন্দোলন নিয়ে জ্ঞানবাবারা এখন খুব ভাবছেন-টাবছেন। ‘যুক্তিবাদ’ নিয়ে অফুরন্ত ধারায় জ্ঞান বিতরণ করে চলেছেন। কারা খাঁটি যুক্তিবাদী, কারা যুক্তিবাদের পথিকৃৎ, সে বিষয়ে ওঁরা নিদান দিচ্ছেন। নিদানটা বড়ই বিচিত্র। ধর্মের ও ঈশ্বরের জায়গাটা সুরক্ষিত রেখে তারপর যাঁরা বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের জয়গান গেয়েছিলেন, গেয়ে চলেছেন, তাঁরাই এইসব বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীর বিবেচনায়—একেবারে খাঁটি যুক্তিবাদী।
এইসব জ্ঞানবাবারা ঈশ্বর বিশ্বাসী এবং বিপরীত চিন্তায় সহাবস্থানকারী পাশ্চাত্যের অতীতের কিছু চিন্তাবিদকে ‘যুক্তিবাদের জন্মদাতা’, ‘যুক্তিবাদী চিন্তার পথিকৃত’ ইত্যাদি বিশেষণ সহযোগে লাগাতারভাবে জনগণের সামনে পেশ করে চলেছেন। আড়কাঠির নির্দেশ মেনে এমন বক্তব্য পেশ করার অধিকার তাঁদের অবশ্যই আছে। ধর্মে-ঈশ্বরে-যুক্তিবাদের জয়গানে সহাবস্থান করা বর্তমানের সংগঠনগুলোর দু’বাহু তুলে গুণকীর্তন করার গণতান্ত্রিক অধিকার তাঁদের আছে। নীতিবোধকে বিক্রি করে দিয়ে অবস্থান পাল্টে সুবিধাবাদী হওয়ার অধিকার তাঁদের আছে। সেই পবিত্র গণতান্ত্রিক অধিকারকেই তাঁরা কিছুদিন হল লাগাতারভাবে প্রয়োগ করে চলেছেন।
বিষয়টি স্পষ্টতর করতে একটি উদাহরণ আপনাদের সামনে পেশ করছি। পেশ করছি এক ‘পত্রবীর জ্ঞানবাবা’র কিছু ‘জ্ঞানগর্ভ’ বক্তব্য। এটি প্রকাশিত হয়েছিল ‘আজকাল’ পত্রিকায় ২৯ জুলাই ১৯৯৫।
“সপ্তদশ শতাব্দীতে গণিতবিদ রেনে দেকার্তের মননে প্রথম জন্ম নেয় যুক্তিবাদ। গ্যালিলিও গ্যালিলাই ঠিক এই সময়েই তাঁর ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন যা যুক্তিবাদকে একটা শক্ত জমির উপর দাঁড় করায়। দেকার্তের পর বেনেডিক্ট স্পিনোজা এবং তাঁর মসাময়িক লিবনিজ এবং তারও পরবর্তীকালে অষ্টাদশ শতকে এমানুয়েল কাণ্ট ও হেগেলের বিশ্ববীক্ষার পথ ধরেই আন্তর্জাতিক যুক্তিবাদ বিস্তারিত এবং বিকশিত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে ফায়ারবাখও তুলে ধরেছেন যুক্তিবাদী তথা র্যাশানলিস্ট আন্দোলনের ধ্বজা। এমনকি ফরাসি যুক্তিবাদের জনক হিসেবে অষ্টাদশ শতাব্দীর ভলতেয়ারকেও গণ্য করা হয়।”
আধুনিক অর্থে এঁরা কেউই যুক্তিবাদী ছিলেন না। দেকার্তে ঈশ্বরের ও আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। গ্যালিলিও ঈশ্বরের সঙ্গে জ্যোতিষ শাস্ত্রেও পরম বিশ্বাসী ছিলেন। স্পিনোজার দর্শন-ও ছিল ঈশ্বর-অস্তিত্বকে সঙ্গী করেই। লিবনিজ তাঁর দর্শনে সমর্থন জানিয়েছিলেন ঈশ্বর ও আত্মা বিষয়ক ধর্মীয় মতবাদকে। কাণ্ট ঈশ্বর ও আত্মার সঙ্গে অতীন্দ্রিয় ব্যাপার-স্যাপারে বিশ্বাসী ছিলেন। হেগেলীয় দর্শনের বুনিয়াদও ছিল ভাববাদী বা অলীক-কল্পনাবাদী। ভলতেয়ারও স্পষ্টতই ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন। এইসব বিশিষ্ট দার্শনিক ও ব্যক্তিত্বরা তাঁদের সময়ে অনা অনেকের থেকেই চিন্তার ক্ষেত্রে এগিয়ে ছিলেন; ধর্মগ্রন্থের ও ধর্মগুরুদের কিছু কিছু যুক্তি-বিরোধী বক্তব্যের বিরোধিতা করেছিলেন, একথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেও আমরা বলতে পারি—কিন্তু তাই বলে ওঁদের ভাববাদী প্রবল চিন্তার দিকটাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে ‘যুক্তিবাদী’ বলে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টাকে কোনওভাবেই সমর্থন করা যায় না।
এমন একটা তথ্যগত ভুলে ভরা পাতি বাজে লেখা বুঝিবা অসতর্কতায় প্রকাশিত হয়ে গেছে, ভেবে আমাদের সমিতির তরফ থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক দেবাশিস ভট্টাচার্য এবং ‘ভারতের মানবতাবাদী সমতি’র অন্যতম সম্পাদক সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায় ‘আজকাল’-এ দুটি চিঠিও দিয়েছিলেন। চিঠি দুটিতে প্রকাশিত বক্তব্যকে খণ্ডণ করে অতি স্পষ্ট করে দেখানো হয়েছিল ষড়যন্ত্রের এক আভাসকে। চিঠি দুটি রেজিষ্ট্রি ডাকেই পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু আমাদের জন্য আরও কিছু বিস্ময় বুঝিবা অপেক্ষায় ছিল। চিঠি দুটি প্রকাশিত হয়নি। পত্র না ছাপবার গণতান্ত্রিক অধিকার পত্রিকার আছে। সেই গণতান্ত্রিক অধিকার তাঁরা একটুও শিথিল হতে দেননি। এই অধিকার রক্ষার মধ্য দিয়ে এটুকু অবশ্য আমাদের ভাবার সুযোগ দিয়েছে, তথাকথিত এইসব বুদ্ধিজীবীদের এ’জাতীয় হাস্যকর লেখার পিছনে তাদের সমর্থন আছে।
তা, সমর্থন থাকতেই পারে, আর পাঁচটা পত্রিকার থেকে তাদের আলাদা করে ‘বিপ্লবী’ বা ‘প্রগতিশীল’ ইত্যাদি বলে কখনই আমরা ভাবিনি। কারণ, এই পত্রিকার পিছনেও মূলধন খাটছে কোটিপতি ব্যবসায়ীর। তাঁর কাছে আর পাঁচটা ব্যবসার মতই এটাও একটা ব্যবসা। কাস্টমার ধরার জনা প্রগতিশীলতার মুখোশ মুখে সাঁটা হয়েছে মাত্র। আর সম্পাদক থেকে সাংবাদিক প্রত্যেকেই মালিকের আজ্ঞাবহ কর্মচারী মাত্র। এঁরা স্বাধীন মালিকের পরাধীন কর্মচারী।
আমাদের কাছেও আমরা পরিস্কার। আমরা চাই প্রতিটি প্রচার মাধ্যমকে ব্যবহার করে আমাদের মতাদর্শকে সবচেয়ে বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে।
এমন একটি উদাহরণ কেউ দেখাতে পারবেন না, যেখানে আমাদের দিয়ে প্রচার মাধ্যম এই সমাজ কাঠামোর স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষে কিছু বলাতে পেরেছেন বা লেখাতে পেরেছেন।
O
এমন একটি উদাহরণ কেউ দেখাতে পারবেন না, যেখানে আমাদের দিয়ে প্রচার মাধ্যম এই সমাজ কাঠামোর স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষে কিছু বলাতে পেরেছেন বা লেখাতে পেরেছেন।
O
‘জ্ঞানবাবা’ চিহ্নিত যুক্তিবাদীরা আধুনিক যুক্তিবাদের মাপকাঠিতে যুক্তিবাদী কিনা, এই প্রসঙ্গ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনায় ঢুকতে আধুনিক যুক্তিবাদ কী, তা এখানে বোঝাতে বসব না। ‘যুক্তিবাদ’ প্রসঙ্গে যাঁরা বিস্তৃত জানতে ইচ্ছুক, তাঁদের অনুরোধ করব, ‘অলৌকিক নয়, লৌকিক’-এর চতুর্থ খণ্ডে অথবা ‘সংস্কৃতিঃ সংঘর্ষ ও নির্মাণ’ গ্রন্থে চোখ বোলাতে।
যাঁরা বিভিন্ন দর্শন নিয়ে পড়াশুনো করেননি, ‘যুক্তিবাদ’ বিষয়ে ভাসা-ভাসা কিছু শুনেছেন, সেই আমজনতাও তাঁদের সাধারণ বোধবুদ্ধির সাহায্য নিয়েই বুঝে নিতে পারবেন, কিছু যুক্তিহীন বিশ্বাসের বিরোধিতার পাশাপাশি কিছু যুক্তিহীন বিশ্বাসকে মেনে নেওয়া আর যাই হোক, যুক্তিবাদী মানসিকতার লক্ষণ নয়। দর্শন সম্পর্কে অতি অল্প জানা মানুষও জানেন, আলোচ্য ওইসব দার্শনিকদের কেউই আধুনিক অর্থে ‘যুক্তিবাদী’ ছিলেন না।
সাধারণ বুদ্ধির মানুষদের যা জানা, তা কি এইসব বুদ্ধিজীবী জ্ঞানবাবাদের অজানা?
একজন ‘জ্ঞানবাবা’ এমনটা লিখলে না হয় সেটা তাঁর অজ্ঞানতা বলে ভাবার অবকাশ থাকলেও বা থাকতে পারত। কিন্তু তা তো নয়! সাম্প্রতিক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা-পত্তর চোখ বোলালেই দেখতে পাব এমন হাস্যকর মিথ্যে একগুচ্ছ ‘জ্ঞানবাবা’দের কলম থেকে নিঃসারিত হয়েই চলেছে।
কেন এমন ছেলেমানুষী মিথ্যে প্রচার করা হচ্ছে? উদ্দেশ্যহীন কোনও পাগলামী কি প্রচার মাধ্যমগুলোতে ভর করেছে? নাকি এর পিছনে রয়েছে কোনও গভীর গোপন উদ্দেশ্য?
কেউ কেউ এর পিছনে উদ্দেশ্যের পরিবর্তে লেখকদের অজ্ঞতাকে দায়ী করতে পারেন। কিন্তু এসব লেখা যে অজ্ঞতার ফলশ্রুতি নয়, তারই একটা প্রমাণ আপনাদের সামনে তুলে দিচ্ছি।
স্পিনেজো থেকে হেগেলকে যুক্তিবাদী বলে ‘আজকাল’ পত্রিকায় সোচ্চার হওয়া এই লেখকটি ১৯৯২ সালের যুক্তিবাদী পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় স্পিনোজা থেকে হেগেলকে ভাববাদী দার্শনিক হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন।
মাত্র তিন বছরে কী এমন হল যে ‘পত্রবীর’ বাবুটিকে ডিগবাজি খেতে হল?
বাবু-বিপ্লবীটির গভীর গোপন ষড়যন্ত্র বুঝতে কোনও অসুবিধে হয় না, যখন দেখি তিনি ‘আজকাল’-এর ওই লেখাটিতেই জানাচ্ছেন, “কার্ল-মার্কস তাঁর দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন কাণ্ট, হেগেল এবং ফয়ারবাখকে দুরন্ত খণ্ডণের মধ্য দিয়ে।”
অর্থাৎ, লেখক পাঠক-পাঠিকাদের মগজে ঢোকাতে চাইলেন—যুক্তিবাদের এইসব পীর-পয়গম্বরদের কুযুক্তিকে খণ্ডন করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কাল মার্কসের বস্তুবাদী দর্শন। অর্থাৎ কার্ল মার্কসের দর্শন ছিল যুক্তিবাদ বিরোধী। কিন্তু বলাই বাহুল্য, মার্কসীয় দর্শন যুক্তিবাদের পথ ধরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
এই জ্ঞানদানকারী লেখক নিঃসঙ্গ নন। সঙ্গী আরও অনেক জ্ঞানবাবা’ই এই একই নিপাট মিথ্যে প্রচার করে চলেছেন।
ওই লেখক ‘আজকাল’-এর এই লেখাটিতে শুধু এপর্যন্ত বলেই কিন্তু থেমে থাকেননি। আরও একটু এগিয়ে বলেছেন—অনেক ক্ষেত্রেই যুক্তিবাদী আন্দোলন আখেরে বুর্জোয়া মতাদর্শকে শক্তিশালী করবে।
এতক্ষণে ঝুলি থেকে বেড়াল বেরুল! মজাটা হল, এই একই ধরণের বক্তব্য অনেক ‘জ্ঞানবাবা’দের কণ্ঠে ও কলমে সম্প্রতি উৎসারিত। উদ্দেশ্য স্পষ্ট। অসাম্যের সমাজ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে যুক্তিবাদী চিন্তার আগ্রাসনকে ঠেকানো। এই ষড়যন্ত্রের আর এক অগ্রণী অংশীদার দেড় যুগ জেল খেটে আপসের রোদে গায়ের টুকটুকে লালকে এখন গোলাপী করার সুবাদে সব রকম লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে গর্বিত ঘোষণা রাখেন, “ইসলাম ইজ দ্য কমিউনিজম অব টুয়েণ্টিফার্স্ট সেঞ্চুরি।” [কোরক সাহিত্য পত্রিকা, মে-আগস্ট, ‘৯৫ সংখ্যা, দ্বিতীয় পর্ব, পৃষ্ঠা-৩৬]
এই মৌলবাদী ‘গোলাপী জ্ঞানবাবা’ তাঁর সাম্প্রতিক একটি লেখায় আর একটি বিস্ফোরক ঘোষণা রেখেছেন—যুক্তিবাদ যে বুর্জোয়া মতাদর্শকেই টিকিয়ে রাখে, তাই নিয়ে একটি বই লিখবেন।
‘যুক্তিবাদ’-এর প্রবল জয়যাত্রাকে রুখতে পরিকল্পনা মাফিক এইসব সুবিধাবাদী জ্ঞানবাবাদের দিয়ে একদিকে বলানো হচ্ছে—’যুক্তিবাদ’ বুর্জোয়া মতাদর্শকে টিকিয়ে রাখে, মার্কস যুক্তিবাদের পথিকৃৎদের দর্শনকে দুরন্ত খণের মধ্য দিয়ে তাঁর দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর এক দিকে তাঁদের এই বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনে ‘না-যুক্তিবাদী’দের ‘যুক্তিবাদী’ বলে প্রচার চালানো হচ্ছে। শুধু তাই নয়, যেসব সংগঠন ধর্মের ও ঈশ্বরের অস্তিত্বকে সুরক্ষিত রেখে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের জয়গান গাইছে, তাদেরকে ‘যুক্তিবাদী’ আন্দোলনের শরিক সংগঠন হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। অথচ নিচ্ছিদ্র নিরীশ্বরবাদিতা-বস্তুবাদিতা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রতি একনিষ্ঠতা, আধুনিক যুক্তিবাদের লক্ষণ। ‘জ্ঞানবাবা’রা অধুনা যে’সব ব্যক্তি ও সংস্থার গায়ে যুক্তিবাদী শিলমোহর দেগে দিচ্ছেন, তাঁদের সবার মধ্যেই আধুনিক যুক্তিবাদের লক্ষণ অনুপস্থিত।
O
যেসব সংগঠন ধর্মের ও ঈশ্বরের অস্তিত্বকে সুরক্ষিত রেখে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের জয়গান গাইছে, তাদেরকে ‘যুক্তিবাদী’ আন্দোলনের শরিক সংগঠন হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। অথচ নিচ্ছিদ্র নিরীশ্বরবাদিতা-বস্তুবাদিতা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রতি একনিষ্ঠতা, আধুনিক যুক্তিবাদের লক্ষণ।
O
মজাটা হল, এইসব তথাকথিত যুক্তিবাদীদের স্বরূপ চিনিয়ে দিতে গেলেই জ্ঞানবাবারা ও তাঁদের আড়কাঠি বেজায় রকম চেঁচামেচি শুরু করে দেন—“কাদা ছোঁড়া-ছুঁড়ি হচ্ছে” বলে। জ্ঞানবাবারা যখন ‘না-যুক্তিবাদী’-দের যুক্তিবাদী বলেন, দেশি-বিদেশি টাকা খাওয়া বিজ্ঞান আন্দোলনকে, মতাদর্শহীন সরকারের লেজুড় বিজ্ঞান আন্দোলনকে, সব্জী সংরক্ষণে মাতোয়ারা বিজ্ঞান আন্দোলনকে, আড্ডায় পরিণত নপুংসক বিজ্ঞান আন্দোলনকে স্পষ্ট-লাইটের আলো ফেলে আলোকিত করার ষড়যন্ত্রে মাতেন, তখন তাঁরা সার্বিক যুক্তিবাদী আন্দোলনকে কী ছুঁড়ে দেন? বেইমানি। স্রেফ বেইমানি। শুধু যুক্তিবাদী আন্দোলনের প্রতি নয়, সমাজের কোটি-কোটি শোষিত মানুষদের প্রতি বেইমানি ছুঁড়ে দেন।
এককালের ‘আগুন খাওয়া’ বিপ্লবীদের বর্তমানে এমন উল্টো-পাল্টা লেখার গণতান্ত্রিক অধিকার আছে। নিজেদের বিপ্লবী মূল্যবোধকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠাবার অধিকার আছে। ধর্মে-মার্কসবাদে-যুক্তিবাদে খাবলা খাবলা অবস্থান করার অধিকার আছে। অসাম্যের এই সমাজ কাঠামোকে সমর্থন জানাবার অধিকার আছে। যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার, কুৎসা ছড়াবার, স্ববিরোধিতায় ভরা হাস্যকর মিথ্যে লেখার অধিকার আছে। ‘জ্ঞানবাবা’র ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার অধিকার আছে।
প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, আপনার-আমার-আমাদেরও অধিকার আছে এঁদের যুক্তিবাদী আন্দোলনের শত্রু, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের শত্রু, সাম্যের সুন্দর সমাজের শত্রু এবং শোষক ও শাসক শ্রেণীর দালাল হিসেবে চিহ্নিত করার ও ঘৃণা করার।
পরিকল্পনা বিবিধ। এক: যুক্তিবাদী আন্দোলনের পাল থেকে হাওয়া কাড়া। দুই: যুক্তিবাদকে বুর্জোয়া মতাদর্শের সহায়ক প্রমাণ করতে প্রয়োজনীয় কিছু সংস্থা ও ব্যক্তিকে তুলে আনো।
এই অসাম্যের সমাজ কাঠামোকে ভাঙার চেষ্টা অনেকবার হয়েছে। বারুদের গন্ধ ভাসিয়ে, রক্তের হোলি খেলে সুন্দর সমাজের স্বপ্ন দেখা অনেক কচি-সবুজ দামাল প্রাণ এখন ঘাসের তলায় ঘুমোচ্ছেন। তাঁদের কর্মকাণ্ড ব্যর্থ হয়নি। বরং তৈরি করে গিয়েছিলেন উত্তরণের সোপানের প্রয়োজনীয় কিছু ধাপ। আমরা শিখেছি—বিপ্লবের আগে, বিপ্লবের সময়, বিপ্লবের পরে, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কোনও বিকল্প নেই। আমরা শিখেছি—এই অসাম্যের সমাজ কাঠামোকে ধাক্কা দিতে হলে, ভাঙতে হলে প্রথমেই অতি স্পষ্টভাবে বুঝে নিতে হবে—এই সমাজ কাঠামোর নিয়ন্ত্রক শক্তি কে? কারাই বা তার সহায়ক শক্তি।
’৯৩-এর জানুয়ারিতে প্রকাশিত হল, ‘সংস্কৃতিঃ সংঘর্ষ ও নির্মাণ।’ অসাধারণ সুন্দর এক সাম্যের সমাজ গড়ে তোলা ও তাকে ধরে রাখার ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রয়োজন বোঝাতে, ইতিহাসের প্রয়োজনে বইটির প্রকাশ ঘটেছিল। বলতে পারা যায়, বইটি ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির ‘ম্যানিফেস্টো’।
বইটি রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যুক্ত কর্মী এবং সচেতন পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগাল। এই প্রথম বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রথম শ্রেণীর নেতারা প্রকাশ্যে দলীয় কর্মী সমাবেশে যুক্তিবাদী সমিতির লাইন মেনে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন। সি. পি. আই (এম) দলের রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু তাঁদের গণসংগঠনের দলীয় কর্মী সম্মেলনে একথাও বললেন, সাক্ষরতা আন্দোলনের চেয়েও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি।
’৯৫-এর জানুয়ারিতে প্রকাশিত হল, ‘অলৌকিক নয়, লৌকিক’ গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ড। এই গ্রন্থে স্পষ্ট ও গভীরভাবে আলোচনা করে দেখানো হল আধুনিক কালের অসাম্যের সমাজ কাঠামো বা ‘সিস্টেম’-এর নিয়ন্তা কে? কারাই বা নিয়স্তার সহায়ক শক্তি। সাম্যের সমাজ গড়ার লক্ষ্যে পৌঁছতে এএক বিরাট অগ্রগামিতা, প্রয়োজনীয় উল্লম্ফন।
সমাজ কাঠামোকে আঘাত হানতে আন্তরিক বিভিন্ন রাজনীতিক ও রাজনৈতিক দল বইটির প্রকাশকে ঐতিহাসিক বলে অভিনন্দিত করলেন। তাঁরা উদ্দীপ্ত হলেন। তারই পাশাপাশি এই সমাজ কাঠামোর নিয়ন্তক শক্তি ধনকুবের গোষ্ঠী ও তাঁদের সহায়ক রাজনীতিক-পুলিশ-প্রশাসন-প্রচার মাধ্যম ও বুদ্ধিজীবীরা ভয়ে কেঁপে উঠলেন।
O
প্রায় প্রতিটি সমাজসেবী সংগঠন বা নন গভর্নমেণ্ট অর্গানাইজেশন, অথবা সংক্ষেপে এন. জি. ও. যখন সরকার ও বিদেশি অর্থ সাহায্যে পুষ্ট এবং প্রায় ক্ষেত্রেই যখন সংগঠনগুলোর পরিচালকরা ওই অর্থ ভাণ্ডারকে আপন পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দে ব্যয় করে চলেছেন, তখন যুক্তিবাদী সমিতি প্রথা ভেঙে সংসার খরচ ছেটে সেই পয়সা খরচ করে দেশের অন্যতম বৃহত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটি চালাচ্ছে।
O
গত কয়েক বছরে ‘যুক্তিবাদ’-এর বিশাল উত্থানে জনগণকে সমাবেশিত করার শক্তিতে সরকার শঙ্কিত হয়েছে। অন্য যে কোনও সমাজসেবী সংগঠনের সঙ্গে আমাদের সমিতিকে এক করে দেখতে না পারাও বোধহয় শঙ্কার একটি কারণ। প্রায় প্রতিটি সমাজসেবী সংগঠন বা নন গভর্নমেণ্ট অর্গানাইজেশন, অথবা সংক্ষেপে এন. জি. ও. যখন সরকার ও বিদেশি অর্থ সাহায্যে পুষ্ট এবং প্রায় ক্ষেত্রেই যখন সংগঠনগুলোর পরিচালকরা এই অর্থ ভাণ্ডারকে আপন পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দে ব্যয় করে চলেছেন, তখন যুক্তিবাদী সমিতি প্রথা ভেঙে সংসার খরচ হেঁটে সেই পয়সা খরচ করে দেশের অন্যতম বৃহত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটি চালাচ্ছে। নিজেদের পকেটের টাকায় চালানো সংগঠন যদি জনমানসকে এই সমাজ কাঠামোর বিরুদ্ধে সমাবেশিত করতে থাকে, তাহলে বাস্তবিকই ভয়ের। সমাজের নিয়ন্ত্রক শক্তি ও তাঁদের সহায়কদের পক্ষে ভয়ের। ওঁরা ভাড়াটে আন্দোলনকারীদের ভয় করেন না। ভয় করেন আদর্শে পরিচালিতদের।
গত কয়েক বছর ধরেই কেন্দ্রীয় সরকারের গোয়েন্দা দপ্তরগুলোর অন্যতম সি, বি. আই. যুক্তিবাদী সমিতি’র কাজকর্মে নজরদারি করছিল। ফাইল খুলেছিল | রাজ্য সরকারের গোয়েন্দা দপ্তর আই, বি’র উপর দায়িত্ব রয়েছে আমাদের উপর নজরদারির। সেখানেও ফাইল খুলেছে। ‘সিস্টেম’-এর বিশ্লেষণ প্রকাশিত হতেই নজরদারির পরিধি ও ব্যাপকতা বিস্তৃত করা হল। সেইসঙ্গে যুক্তিবাদের আগ্রাসন রুখতে, তাদের পা-টা আঘাত হানতে অগ্রণী ভূমিকা নিল প্রচার মাধ্যম ও বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশ। পরিকল্পনাকে সার্থক করতে দুটি লক্ষ্য স্থির করল। এক: প্রকৃত যুক্তিবাদী আন্দোলনের পাল থেকে হাওয়া কেড়ে নিতে মেক বিজ্ঞান আন্দোলনকে ‘স্পনসর করা, প্রচারের আলোকে তুলে এনে আমজনতা ও আন্দোলনকারীদের বিভ্রান্ত করা। দুই: যুক্তিবাদ’কে বুর্জোয়া মতাদর্শের সহায়ক প্রমাণ করতে এমন সংস্থা ও ব্যক্তিকে তুলে আনা ও প্রজেক্ট করা, যারা একই সঙ্গে ঈশ্বরতত্ত্ব ও যুক্তিবাদের পক্ষে জয়ধ্বনি দেয়, যাদের তাগা-তাবিজ শোভিত বাহু যুক্তিবাদের পক্ষে আস্ফালন করে। এ সেই পুরনো কৌশল। এ সেই নকশালবাড়ি আন্দোলনে উদ্দীপ্ত আদর্শের মধ্যে সমাজ-বিরোধী ঢুকিয়ে ‘নকশাল = সমাজবিরোধী প্রমাণ করার মতই এক গভীর ষড়যন্ত্র।
আমরা জানি, ‘যুক্তিবাদী’ শব্দটা কারও একচেটিয়া নয়। ‘যুক্তিবাদ’ নিয়ে আন্দোলন করাটাও কারও একচেটিয়া নয়। তার-ই সঙ্গে এও মনে করি, অন্যান্য যুক্তিবাদী সংস্থা বা যুক্তিবাদ নিয়ে আন্দোলনে সামিল (!) সংস্থাগুলোর সঙ্গে আমাদের স্পষ্ট মতাদর্শগত যে পার্থক্য আছে, সেগুলো আন্দোলনের স্বার্থেই সাধারণের কাছে তুলে ধরা উচিত। ‘যুক্তিবাদ’-এর সংজ্ঞাও এইসব সংস্থার চোখে ভিন্নতর। এদের চোখে ‘যুক্তিবাদ’ একটি সামগ্রিক জীবনদর্শন হয়ে ওঠেনি। হয়ে ওঠেনি সাংস্কৃতিক আন্দোলন। এদের কাছে যুক্তিবাদ শুধু বিচার-বিশ্লেষণের কিছু পদ্ধতিগত কায়দা-কানুন ও কিছু কিছু কুসংস্কারের বিরূদ্ধে প্রচার। এরা ‘যুক্তিবাদ’ বলতে কী বোঝেন? কেমনভাবে বোঝেন? আসুন দু’চার কথায় বুঝে নিই। সংগঠনগুলোর সংগঠকদের প্রকাশিত বক্তব্যের মধ্য দিয়েই বুঝে নিই। প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, তারপর আপনারাই ঠিক করবেন, আপনাদের ‘সমর্থন’, ‘অসমর্থন’ কোন পক্ষে যাবে। আমরা অতি আন্তরিকতার সঙ্গে বিশ্বাস করি, ‘জনগণই শেষ কথা বলেন’। আর এই পরম বিশ্বাসই আমাদের বেঁচে থাকার শ্বাস-প্রশ্বাস, অসাম্যের শক্তিশালী সমাজ কাঠামোর বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণা।
ভারতীয় যুক্তিবাদী সংসদ
প্রতিষ্ঠা ১৯৯৪ সালে। প্রতিষ্ঠাতা নেতারা প্রত্যেকেই পশ্চিমবঙ্গের একটি জব্বর মার্কসবাদী রাজনৈতিক দলের বা তার কোনও না কোনও গণসংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। রাজনৈতিক দলটি ইতিমধ্যেই বিজ্ঞান আন্দোলন ও যুক্তিবাদী আন্দোলনে জনগণকে সামিল করতে একটি ‘বিজ্ঞান মঞ্চ’ খুলেছে। তারপর একই কাজে বকলমে আবার একটা গণসংগঠন খোলা—একটি নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত। যুব-ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক-মহিলা-রাজ্যসরকারী কর্মচারী-লেখক-শিল্পী ইত্যাদি প্রত্যেকটি পরিধিতে কাজ করতে রাজনৈতিক দলটির একটি করেই গণসংগঠন। শুধুমাত্র বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ নিয়ে আন্দোলনের ক্ষেত্রে দুটি গণসংগঠন কেন? রাজনৈতিক দলটি রাজ্যসম্মেলনে স্বীকার করেছে, বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে জনগণের উপর তাদের গণসংগঠনের প্রভাব খুবই সামান্য।
‘ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি’ বিজ্ঞান আন্দোলনকে বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ গড়ার আন্দোলন হিসেবে জনমানসকে প্রভাবিত করায় এবং যুক্তিবাদী আন্দোলনে জনগণকে বিশালভাবে সমাবেশিত করে মূলস্রোত তৈরি করায় সরকারি বা বিদেশি সাহায্য পুষ্ট কোনও ভাড়াটে আন্দোলকদের পক্ষে আমাদের পাল থেকে হাওয়া কেড়ে নেওয়া ছিল একান্তই অসম্ভব। তাই কি আমাদের সমিতির কাছাকাছি নাম রাখা হয়েছে জনগণকে বিভ্রান্ত করে ফায়দা তুলতে?
‘ভারতীয় যুক্তিবাদী সংসদ’-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ডঃ বেলা দত্তগুপ্তের কুসংস্কার প্রসঙ্গে রাখা একটি সাম্প্রতিক বক্তব্যের দিকে প্রিয় পাঠক-পাঠিকাদের নজর আকর্ষণ করছি।
“শিশুদের কোমরে তামার পয়সা বাঁধার চল আমাদের দেশে দীর্ঘদিন ধরে রয়েছে। অনেকেই তা কুসংস্কার বলে চিহ্নিত করেন। কিন্তু একথা এখন চিকিৎসাশাস্ত্রে সর্বজনবিদিত যে মানুষের দেহে তামা একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ধাতু এবং সুস্থ স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য তা অত্যন্ত দরকারও। তাই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে গিয়ে অনেক সময়ই যা বলা হয় তা নিতান্তই অসার, অনেকটাই বৃটিশদের কাছ থেকে যান্ত্রিকভাবে ধার করা চিন্তার পরিণতি।”
বক্তব্যটি প্রকাশিত হয়েছিল ২ সেপ্টেম্বর ‘৯৪-এর ‘যুগান্তর’ দৈনিক পত্রিকায়। যে প্রতিবেদনে বক্তব্যটি প্রকাশিত হয়েছিল, তার লেখক ভারতীয় ‘যুক্তিবাদী সংসদ’-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক শমিত কর। অতএব বক্তব্য বিকৃত করার অভিযোগ এখানে খাটে না।
আসুন, এবার আমরা দেখি ডঃ দত্তগুপ্তের বর্ণিত ‘চিকিৎসাশাস্ত্রে সর্বজনবিদিত’ বাস্তবিকই কতটা ‘সর্বজনবিদিত’।
তারিখটা ২৬জুন। সাল ১৯৮৬। কলকাতার রাজাবাজারে অবস্থিত ‘সাইন্স কলেজ’-এ দীর্ঘ আলোচনার পর ভারতের বিশিষ্ট ১৮ জন বিজ্ঞানী একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। প্রস্তাবটির একটি অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি:
“আমাদের শরীরে রক্ত আছে। প্রয়োজনে বাহির হইতে সংগ্রহ করিয়া রক্ত দেওয়া হয়। কিন্তু কোনও ব্যক্তি যদি হঠাৎ দাবি করিয়া বসেন পশু বা মানুষের রক্ত গায়ে মাখিয়াই শরীরের রক্তস্বল্পতা দূর করা সম্ভব, তাহা হইলে তাহার মানসিক সুস্থতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। কেহ যদি প্রশ্ন করিয়া বসেন রক্তস্বল্পতার ক্ষেত্রে চিকিৎসাশাস্ত্রে আয়রণ ট্যাবলেট-ক্যাপসুল ইত্যাদির প্রয়োগবিধি আছে, অতএব লৌহ-আংটি ধারণে ওই একই কার্য সমাধা হইবে না কেন? তবে প্রশ্নকর্তার কাণ্ডজ্ঞান বিষয়ে সন্দিহান হই। এইরূপ প্রশ্নকর্তা তাঁহার নিজের রক্তস্বল্পতা দেখা দিলে ভারি লৌহখণ্ড শরীরের সর্বত্র বাধিয়া রাখিয়া পরীক্ষা করিলেই তাঁহার প্রশ্ন ও বক্তব্যের অসারতা বুঝিতে পারিবেন।”
এই বিষয়ে পূর্ণ প্রস্তাব জানতে দেখতে পারেন, ‘অলৌকিক নয়, লৌকিক’ গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে।
এতো গেল বিজ্ঞানীদের সর্বজনবিদিত বক্তব্য, বিজ্ঞানের বক্তব্য। তা বিজ্ঞানবিরোধী বক্তব্য রাখার অধিকার ভারতীয় যুক্তিবাদী সংসদের সভাপতির নিশ্চয়ই আছে। তাঁর বক্তব্যকে প্রচার করার অধিকারও যুক্তিবাদী সংসদের আছে। ঘুনসি-তাগা-তাবিজ-ধাতু ও গ্রহরত্ন পরে যুক্তিবাদী আন্দোলন করার গণতান্ত্রিক অধিকারও যুঝিবাদী সংসদের আছে। ওদের কাজ-কর্মের ফল ওদের জন্যই সংরক্ষিত থাকলে আমাদের শিরপীড়ার কোনও কারণ হত না। কিন্তু তা তো হওয়ার নয়! প্রত্যাশা মতই একদিকে কিছু প্রচার মাধ্যম যখন যুক্তিবাদী সংসদের উপর প্রচারের আলো ফেলছে, রামমোহন থেকে কেশবচন্দ্রের মত মহান যুক্তিবাদীদের উত্তরসূরী বলে সাটিফিকেট দিচ্ছে তথাকথিত যুক্তিবাদী দৈনিক পত্রিকা (অবশ্য ‘ভারতীয় যুক্তিবাদী সংসদ’-এর সাধারণ সম্পাদক শ্রীমানিক পাল মহাশয় একটি ইস্তাহার প্রকাশ করে রামমোহন, কেশব সেনকে আমাদের সমাজে বিজ্ঞানমনস্কতা আনার ক্ষেত্রে উজ্জ্বল নক্ষত্র বলে বর্ণনা করেছেন। যদিও রামমোহন থেকে কেশবচন্দ্র ছিলেন ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচারক ও ঈশ্বর বিশ্বাসী), তখন আর এক দিকে প্রচার মাধ্যম তাবিজধায়ী যুক্তিবাদীদের আস্ফালনকে হাসির খোরাক করে কার্টুনে পাতা ভরাচ্ছে (এমনই এক কার্টুন আনন্দবাজার পত্রিকার ‘রবিবাসরীয়’তে প্রকাশিত হয়েছে ২৯ অক্টোবর ১৯৯৫)।
প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, যুক্তিবাদী আন্দোলনকে এমন ভাঁড়ামোতে দাঁড় করানোর জন্য তো আমাদের সমিতি দায়ী ছিল না। তবু যুক্তিবাদী আন্দোলন ষড়যন্ত্রের শিকার হল। আনন্দবাজার পত্রিকার বেশ কিছু পাঠক-পাঠিকাদের চোখে যুক্তিবাদী আন্দোলন ‘ফালতু’ হল। প্রিয় পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির জন্য জানিয়ে রাখি—’ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি’র কেন্দ্রীয় বা কোনও শাখায় কার্যকরী সমিতির সদস্য হওয়ার অনাতম প্রাথমিক ও আবশ্যিক শর্ত, তাবিজ-কবজ-গ্রহরত্ন-ঈশ্বর-আত্মা-ভূত-জ্যোতিষ ইত্যাদিতে বিশ্বাস জাতীয় স্থূল কুসংস্কারের উর্ধ্বে থাকতে হবে, এমনকি কোনও অজুহাতেও গ্রহরত্ন-টত্ন ধারণ করতে পারবেন না।
O
‘ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির কেন্ত্রীয় বা কোনও শাখায় কার্যকরী সমিতির সদস্য হওয়ার অন্যতম প্রাথমিক ও আবশ্যিক শর্ত, তাবিজ-কবজ-হয়-ইর-আত্ম-ভূত-জ্যোতি ইত্যাদিতে বিশ্বাস জাতীয় ফুল কুসংস্কারের উর্ধ্বে থাকতে হবে।
O
‘ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি’র কেন্দ্রীয় বা কোনও শাখায় কার্যকরী সমিতির সদস্য হওয়ার অনাতম প্রাথমিক ও আবশ্যিক শর্ত, তাবিজ-কবজ-গ্রহরত্ন-ঈশ্বর-আত্মা-ভূত-জ্যোতিষ ইত্যাদিতে বিশ্বাস জাতীয় স্থূল কুসংস্কারের উর্ধ্বে থাকতে হবে
সংসদের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমানিক পাল কর্তৃক প্রচারিত সাম্প্রতিক একটি প্রচারপত্র পাঠ করে জানতে পারলাম, ওঁদের সংগঠনটির পুরো নাম, ‘ভারতীয় যুক্তিবাদী সংসদ প. ব.’। এটা তো কোনও সর্বভারতীয় সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কমিটি বা প্রাদেশিক শাখা নয়? তবুও কোনও শাখাহীন, আঙুলে গোনা সদস্য সংখ্যার এই ‘যুক্তিবাদী সংসদ’ নামের আগে ভারতীয় ও পিছনে ‘প. ব.’ অর্থাৎ (সম্ভবত) ‘পশ্চিমবঙ্গ’ শব্দ দুটি কেন জুড়ে দিল? এ আমার কাছে বাস্তবিকই রহস্য! এ যেন ‘জাপানী টেপ-রেকর্ডার, মেড ইন ইণ্ডিয়া’।
ইণ্ডিয়ান র্যাশনালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন
দিল্লীর ঠিকানা অফিস হিসেবে বাবহৃত হয়। প্রধান নেতা এডামারুকু। ওদের ‘র্যাশনালিজম’ বা ‘যুক্তিবাদ’-এ মাঝে-মধ্যে চালেঞ্জ উপস্থিত। অনুপস্থিত অধ্যাত্মবাদ-ধর্ম-ঈশ্বর তত্ত্বের বিরোধিতা।
সম্প্রতি কিছু প্রচার মাধ্যমের মধ্যে ওদের শক্তিকে ফাঁপিয়ে দেখাবার প্রবণতা লক্ষ্য করছি। সংগঠন ছোট কি বড় তাতে কিছুই এসে যায় না, আমরা জানি। সুবিধাবাদী রাজনৈতিক দলগুলোর বিশাল আকার আমরা দেখেছি। আবার এমনও দেখেছি আদর্শের চারাবট এখন বনস্পতি—হাতের কাছেই উদাহরণ। দশ বছরে একটা মানুষ লক্ষ মানুষ হয়েছে। আমরা দেখেছি। অতএব এক থাকাটা তত্বগতভাবে কখনই গুণগতমানের দৈন্য প্রকাশ করে না। কিন্তু দীনতা প্রকাশ করে সেইসব প্রচার-মাধ্যমগুলোর, যারা এক’কে ফাঁপিয়ে লক্ষ করার চেষ্টায় মেতেছেন। এই দীনতারই আর এক নাম ‘হলদে সাংবাদিকতা’।
বি. বি. সি-র চ্যানেল ফোরের জন্য ভারতের যুক্তিবাদী আন্দোলন নিয়ে ছবি তুলতে ‘৯৪-এ তিন দফা ভারত সফরে এসেছিলেন ডিরেক্টর, প্রোডিউসর রবার্ট ঈগল। এডামারুকুর সঙ্গে ঈগল যোগাযোগ করলেন। ওঁর সংগঠনের কাজ-কর্মকে ক্যামেরা বন্দি করতে চাইলেন। এডামারুকু জানালেন লোক কই? মাস তিনেক সময় পেলে কয়েকজনকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিতে পারি। শেখালেন। জনা চারেক ছাত্র ও জনা পঞ্চাশ দর্শক জোগাড় করতে মাস তিনেক সময় দিতে হয়েছিল।
সংস্থা আছে। কাজের লোক নেই। স্টাডি ক্লাশ নেই। সহযোদ্ধা তৈরির প্রক্রিয়া নেই। আমাদের চেয়েও অনেক প্রাচীন সংগঠন হওয়া সত্বেও বাস্তবিক পক্ষে এখনও পুরোপুরি কাগুজে সংগঠন।
প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, একবার প্রশ্ন করুন—তবু এইসব কাগুজে সংগঠনকে কেন ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তুলে আনা হচ্ছে? উত্তর আপনি নিজেই পাবেন। সেই দুটি উত্তর। আপনার-আমার-আমাদের উত্তর মিলবেই। সততার সঙ্গে খুঁজলে উত্তর যে এক-ই হবে।
‘যুক্তিবাদী’ শব্দটি নিজেদের নামের সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও বিজ্ঞান আন্দোলন বা যুক্তিবাদী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, কিছু সংগঠন। তাদের চোখে ‘যুক্তিবাদী আন্দোলন’ বা ‘বিজ্ঞান আন্দোলন’-এর সংজ্ঞা কী? সংগঠকদের বক্তব্যের মধ্য দিয়েই বুঝে নিই আসুন।
পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ
জন্ম ১৯৮৬-র নভেম্বরে। একটি মার্কসবাদী রাজনৈতিক দলের শাখা। ‘বিজ্ঞান আন্দোলনের ভূমিকা’ প্রসঙ্গে মঞ্চের সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য, “পরিবেশ দূষণ, রোগ প্রতিরোধ, জলসেচ, মৃত্তিকার পরীক্ষা, কীটনাশকের প্রতিক্রিয়া, পারমানবিক যুদ্ধের ভয়াবহতা, জ্বালানী ও শক্তির সমস্যা ইত্যাদি সময়োপযোগী সমস্যা বিষয়ে মানুষের মধ্যে ক্রমাগত প্রচার চালান বিজ্ঞান আন্দোলনের একটি প্রধান কাজ।”
আরও কাজের মধ্যে বিজ্ঞান প্রদর্শনী, বিজ্ঞান মেলা, মানুষের কাছে বিজ্ঞানের সুযোগ-সুবিধে পৌঁছে দেওয়ার কথা আছে। যেসব কথা আছে সে সব কথা নিশ্চয়ই ভাল। কিন্তু আমাদের সঙ্গে ওদের সংগঠনের মূলগত পার্থক্য বিজ্ঞান আন্দোলনের সংজ্ঞা নিয়েই। ওরা মনে করেন—বিজ্ঞানের সবচেয়ে বেশি সুযোগ-সুবিধে পৌঁছে দেওয়াই বিজ্ঞান আন্দোলন। আমরা মনে করি-বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ গড়ার আন্দোলনই বিজ্ঞান আন্দোলনের লক্ষ্য হওয়া উচিত।
মঞ্চে কিছু বিধি নিষেধও আছে। ধর্মে বিশ্বাসী মানুষদের চোখে ধর্মগুরু ও জ্যোতিষীরা শ্রদ্ধেয়। তাই ধর্মগুরু ও জ্যোতিষীদের বিরুদ্ধে ‘রা’-কাটা বারণ। কারণ এতে করে বিশ্বাসী মানুষদের বিশ্বাসে আঘাত হানা হবে। মঞ্চের লক্ষ্য, জনচেতনাকে উঠিয়ে আনা নয়। জনচেতনার মনে নিজেদের নামিয়ে আনা। নির্বাচন-নির্ভর রাজনৈতিক দলের গণসংগঠন হলে বুঝিবা এভাবেই চলতে হয়। কারণ, ওদের কাছে শেষ পর্যন্ত মানুষকে যুক্তিবাদী করার চেয়ে মানুষের ভোট পাওয়াটাই জরুরী হয়ে ওঠে। আর তাই তো, ওদের সংগঠনে আমজনতাকে সামিল করতে খোলা-মেলা মুক্ত হাওয়া। মঞ্চের আঞ্চলিক স্তর থেকে কেন্দ্রীয় স্তর পর্যন্ত সর্বত্রই তাই পুজোকমিটি-তাগা তাবিজ বিজ্ঞান আন্দোলন ইত্যাদি স্ববিরোধিতা পরম নিশ্চিন্তে সহাবস্থান করে।
‘৯৪-এর কলকতা পুস্তক মেলায় মঞ্চ বইয়ের দোকান দেয়। নানা বইয়ের পাশে কুসংস্কারের ধারক-বাহক বইও স্টলে সহাবস্থান করে। এবং তা যে অনবধানতায় নয়, এটা বুঝতে পারি, যখন আমাদের সমিতির তরফ থেকে তাদের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করার পরও দেখি যথা পূর্বং তথা পরং।
একটি ঘটনা। ১৯৯৩-এর সেপ্টেম্বর। রামকৃষ্ণ মিশন ‘বিশ্ব ধর্ম সম্মেলন’-কে রাজনৈতিক স্টার মেগাস্টারের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির মেলবন্ধনকে নতুন মাত্রা দিতে সচেষ্ট। শহর কলকাতার হোর্ডিংগুলো দাঁড়িয়ে আছে ধর্ম সম্মেলনে রাষ্ট্রনেতাদের উপস্থিতির সদম্ভ ঘোষণা নিয়ে। ভারতীয় সংবিধানে দেওয়া ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’-র ব্যাখ্যাকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করতে রাষ্ট্রীয় পদাধিকারিদের ‘বিশ্ব ধর্ম সম্মেলন’-এ অংশগ্রহণ থেকে বিরত করতে যুক্তিবাদী সমিতি তখন জোরাল আন্দোলন গড়ে তুলেছে। আমাদের সমিতি সম্মেলনে যোগ না দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নেতাদের কাছে, এবং দল ও নেতাদের কাছ থেকে বিপুল সাড়া পেয়ে আমরা বাস্তবিকই আপ্লুত। ঠিক এমনি সময়ে বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনের আহ্বায়ক স্বামী লোকেশ্বরান্দ’র সুরে সুর মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ’-এর সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য প্রকাশিত হলো বাংলা দৈনিক ‘সংবাদ প্রতিদিন’-এর পাতায় (৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩)। মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক আমাদের আন্দোলনের তীব্র বিরোধিতা করলেন। এভাবে তিনি ধর্মের পিঠে জুড়ে দিতে চাইলেন বিজ্ঞানের পাখা।
১৯৯৫ এর ডিসেম্বরে মঞ্চের নেতৃত্বে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ জাঠা অনুষ্ঠিত হলো। খড়গপুরে জাঠার উদ্বোধন হলো ঈশ্বরে প্রার্থনা সংগীতের মধ্য দিয়ে।
গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র
জন্ম ১৯৮৯ সালে। সি. পি. এম. নিয়ন্ত্রিত পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ যখন বিভিন্ন বিজ্ঞান ক্লাবগুলোকে নিজেদের দখলে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে, তখন কিছু বিজ্ঞান ক্লাব ও বিজ্ঞান পত্রিকাগোষ্ঠীর অস্তিত্ব বজায় রাখার তাগিদে গড়ে উঠেছিল এই সময় কেন্দ্র। ঘোষিত কর্মসুচীতে ছিল—কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, গণস্বাস্থ্য আন্দোলন গড়ে তোলা, পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলা সহ আরও অনেক কিছুই।
এক বছর না যেতেই ২৫.৩.৯০ তারিখে ৮ নং সার্কুলার দিয়ে সমন্বয় কেন্দ্র যুক্ত সংগঠনগুলোকে জানাল-অদৃষ্টবাদ, কর্মফল বিশ্বাস, ভূত বা ঈশ্বরজাতীয় বিশ্বাস মানুষের মন থেকে দূর করা দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ব্যাপার। তাই বঞ্চিত মানুষদের কুসংস্কারমুক্ত করার আন্দোলনের এখন কোনও প্রয়োজন নেই। আগে অলৌকিকতা বিরোধী, ঈশ্বরতত্ত্ব বিরোধী, অদৃষ্টবাদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার যে পথ নেওয়া হয়েছিল, তা ছিল ভুল পথ।
গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির লাইনকে পুরোপুরি বর্জন করল। বিজ্ঞান মঞ্চের লাইনকে সমর্থন করল। তারপর-ঈশ্বর বিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখার পক্ষে, অধ্যাত্মবাদকে টিকিয়ে রাখার পক্ষে ওদের কর্ণধারেরা কলম ধরতে লাগলেন।
গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ পত্রিকাগোষ্ঠী ‘উৎস মানুষ’ ১৯৯৪-এর অক্টোবর-নভেম্বর সংখ্যায় ‘যুক্তিবাদ ও যুক্তিবাদীর মুখোমুখি’ শিরোনামের প্রবন্ধে জানাল:
“ভূতের সঙ্গে ঈশ্বরের অস্তিত্বের তুলনামূলক বিচারে গেলে ঈশ্বরবাদীরা হয়ত রুষ্ট হবেন, কারণ, যেখানে বিজ্ঞান নির্ভর যুক্তির প্রবল প্রয়োগে ভূতকে আমরা প্রায় উৎখাত করে এনেছি, সেখানে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিচারে একই ধরণের বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রয়োগ করতে আমরা অস্বস্তি বোধ করি। ঠিক একই সঙ্কোচ বা অস্বস্তির মুখোমুখি আমরা হই দেবমূর্তিকে দেবতাহীন বলে ঘোষণা করতে। এর কারণ আমাদের মজ্জাগত ধর্মীয় সংস্কার। যেহেতু এই সংস্কার সমাজের সার্বিক উন্নয়ন ও আধ্যাত্মিক বোধ উন্মেষের কাজে সাহায্য করে, এই সংস্কারকে আমরা কুসংস্কার বলব না।”
অর্থাৎ, ঈশ্বর বিশ্বাস কুসংস্কার তো নয়ই, বরং এই বিশ্বাস সমাজের সার্বিক উন্নয়নে সাহায্য করে এবং অধ্যাত্মিক বোধ বা আত্মা সংক্রান্ত মতবাদ বিষয়ে বোধের উন্মেষে সাহায্য করে। এরপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।
প্রগতিশীল পত্রিকা হিসেবে পরিচিত ‘অনুষ্টুপ’ পত্রিকা ৯৫’-এর কলকাতা পুস্তক মেলায় বিশেষ বিজ্ঞান সংখ্যা প্রকাশ করল। সেখানে বিজ্ঞানে অবগাহন প্রবন্ধটির উপসংহারে লেখক জানালেন, “বিজ্ঞানমনস্কতা একজন ব্যক্তি মানুষের আত্মিক উন্নতি ও অধিকার আদায়ের সহায়ক শক্তি হতে পারে, কিন্তু নৈতিকতা ছাড়াও আবেগ-অনুভূতির জগতে বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ এখনো স্পষ্ট নয়।…তাই ফের খেয়াল রাখতে হয় বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতায়। বিজ্ঞান মানবপ্রজাতির বহির্জগত ও অন্তর্জগতের সার্বিকমুক্তির মন্ত্র হাতে বসে নেই, বিজ্ঞান কোনো মুক্তিদাতা বা পরমাত্মার বিকল্প নয়।”
প্রবন্ধটির লেখক ‘উৎস মানুষ’ পত্রিকার সম্পাদক। ধরে নিলাম লেখক অনবধানতায় ‘আত্মিক’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আসলে মূল্যবোধ বা ‘নীতিবোধ’-জাতীয় কোনও শব্দ ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। তবু বলব, এই ধরনের ‘ভাববাদী’ শব্দ ব্যবহার বিষয়ে তাঁর আরও একটু সতর্ক থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তারপর? তিনি সরাসরি বিজ্ঞানের বিচরণ ক্ষেত্র নিয়ে ‘লক্ষণের গণ্ডি টানলেন। ভবিষ্যৎ বিষয়েও নিদান দিলেন, বিজ্ঞান সার্বিক মুক্তির পথ হতে পারে না।
বাস্তবে কিন্তু বিজ্ঞানই মুক্তি দেয়। অজ্ঞানতা থেকে মুক্তি। বিজ্ঞানের পথ ধরেই গড়ে ওঠে বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধ। সমাজবিজ্ঞানই আমাদের নৈতিকতা বুঝতে সাহায্য করে এবং গড়তে সাহায্য করে, সাম্যের সমাজ গড়ার পথ দেখাতে পারে। মনোবিজ্ঞান ব্যাখ্যা দিতে পারে আবেগ-অনুভূতির এবং দেয়ও। মানুষের মুক্তি যদি কেউ দিতে পারে, তবে তা বিজ্ঞানই। ‘পরমাত্মা’-জাতীয় কেউ কখনও মুক্তিদাতা নয়। ‘পরমাত্মা’-জাতীয় অতীক চিন্তা বরং শৃঙ্খলিত করে মানুষের মননকে, মানুষের ব্যক্তি সত্তাকে।
বছর কয়েক আগে ‘উৎস মানুষ’ পত্রিকাতে একই সংখ্যায় দুটি বইয়ের সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। একটি অলৌকিক নয়, লৌকিক প্রথম খণ্ডের, আর একটি মার্টিন গার্ডনার-এর ‘সাইন্স: গুড, ব্যাড অ্যাণ্ড বোগাস’। ‘অলৌকিক নয়, লৌকিক’ বইটি যে কত ‘ওঁচা”, কত ‘ভুসি’ মাল তা প্রচুর আবেগের সঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছিল। বইটি যে অনেকের কাছেই বেজায় বাজে লাগে, তা আমার অজানা নয়। সমালোচকের বাজে লাগার অধিকার নিশ্চয় আছে। স্বীকার করি। কিন্তু ‘উৎস মানুষ’-এই করেই থামল না। একই বিষয়ের দুটি বইয়ে কত তফাৎ, দেখাতে ‘মডেল’ বা আদর্শ হিসেবে খাড়া করল মার্টিন গার্ডনারের বইটিকে। ছত্রে ছত্রে আবেগ ঢেলে বোঝাল গার্ডনার কী দারুন যুক্তিবাদী।
গার্ডনার কতখানি যুক্তিবাদী? বোঝাতে শুধু এটুকু বললেই বোধহয় যথেষ্ট হবে, তিনি তাঁর বইতেই স্পষ্ট করে লিখেছেন, তাঁর ঈশ্বর বিশ্বাস ও আত্মায় বিশ্বাস করার কথা। ‘উৎস মানুষ’-এর প্রেরণা পাওয়ার মত আদর্শই বটে! গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্রের এক নেতা ‘গণদর্পণ’ পত্রিকায় (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৯৫ সংখ্যায়) বিভিন্ন স্কুলে ‘ইস্কন’ যে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করছে, সেই প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে লিখলেন—ইস্কনের বিলাস বহুল জীবন চৈতন্যের আদর্শের সঙ্গে মেলে না। ইস্কনের এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে চৈতন্যের আদর্শ ও ঐতিহ্যকে সামনে রেখে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে।
বাঃ! কী সুন্দর যুক্তি! এক অধ্যাত্মবাদী চিন্তার প্রসার রুখতে আর এক অধ্যাত্মবাদী চিন্তার প্রসারের পক্ষে উমেদারি। অর্থাৎ, বিপ্লবী-আনা দেখিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে অধ্যাত্মবাদীদের পক্ষেই নির্ভেজাল দালালি।
আমরা মনে করি, ঈশ্বর বিশ্বসের মত অলীক বিশ্বাসের পক্ষে দালালি করে আর যাই হোক, বিজ্ঞান আন্দোলন করা যায় না, এবং ইস্কনের মত ভাববাদীদের বিরুদ্ধে লড়া যায় না।
প্রচার মাধ্যম ও তার ভূমিকা
সংবাদপত্রের পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে সাধারণভাবে এক ধরনের বিপদজনক ভুল ধারণা রয়েছে। অমুক পত্রিকা প্রগতিশীল, তমুক পত্রিকা প্রতিক্রিয়াশীল ইত্যাদি। ধারণাটা পুরোপুরি ভুল। সংবাদপত্র এবং প্রচারমাধ্যমগুলো তাদের মালিকদের কাছে আর পাঁচটা ব্যবসার মত নিছকই ব্যবসা। উৎপাদন কর, খদ্দের ধর, বিক্রি কর। আর পাঁচটা ব্যবসার মতই এখানেও সাধারণভাবে যত বেশি বিক্রি, তত বেশি লাভ।
O
সংবাদপত্রের পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে সাধারণভাবে এক ধরনের বিপদজনক ভুল ধারণা রয়েছে। অমুক পত্রিকা প্রগতিশীল, তমুক পত্রিকা প্রতিক্রিয়াশীল ইত্যাদি। ধারণাটা পুরোপুরি ভুল। সংবাদপত্র এবং প্রচারমাধ্যমগুলো তাদের মালিকদের কাছে আর পাঁচটা ব্যবসার মত নিছকই ব্যবসা।
O
বড় পুঁজি বিনিয়োগের আগে প্রতিটি শিল্পপতি বিশেষজ্ঞদের দিয়ে সমীক্ষা চালান। প্রাথমিকভাবে বুঝে নেন বাজারের অবস্থা তারপর নামেন উৎপাদনে।
বৃহৎ পত্র-পত্রিকা উৎপাদনের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। সম্ভাব্য পুঁজি বিনিয়োগকারী বিশেষজ্ঞ দিয়ে সমীক্ষা চালান। সমীক্ষকরা কয়েক মাস ব্যাপী সমীক্ষা চালান নানাভাবে, আর একটা বড় অংশ জনমত যাচাই। তারপর তাঁরা রিপোর্ট পেশ করেন। রিপোর্টে পত্রিকার চরিত্র কী কী ধরনের হলে সম্ভাব্য পাঠক কতটা হতে পারে, তার একটা হদিস দেওয়া হয়। এই সমীক্ষা রিপোর্টের ভিত্তিতে পুঁজিপতি ঠিক করেন তার পত্রিকার চরিত্রের রূপরেখা, ঠিক করেন পেপার পলিসি। কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত হন সম্পাদক থেকে সাংবাদিক। এঁরা প্রত্যেকেই বুঝে নেন পত্রিকার চরিত্রের রূপরেখা, এই রূপরেখা ভাঙার কোনও স্বাধীনতাই থাকে না সম্পাদক থেকে সাংবাদিক কারুরই। ‘সংবাদপত্রের স্বাধীনতা’ বলে যে শব্দটি আমরা অহরহ শুনে থাকি, যে শব্দটা নিয়ে ফি-বছর গোটা কয়েক সেমিনার হয় দেশের বড়-মেজ শহরগুলোতে, সেই শব্দটি একটিই মাত্র অর্থ বহন করে; আর তা হলো সংবাদপত্র মালিকের পত্রিকা-চরিত্রকে বজায় রাখার স্বাধীনতা, যা খুশি লেখার স্বাধীনতা, এবং এই স্বাধীনতা নামের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠলে সব সংবাদপত্র মালিকদের সংগঠিতভাবে আঘাত হানার স্বাধীনতা।
O
‘সংবাদপত্রের স্বাধীনতা’ বলে যে শব্দটি আমরা অহরহ শুনে থাকি, যে শব্দটা নিয়ে ফি-বছর গোটা কয়েক সেমিনার হয় দেশের বড়-মেজ শহরগুলোতে, সেই শব্দটি একটিই মাত্র অর্থ বহন করে; আর তা হলো সংবাদপত্র মালিকের পত্রিকা-চরিত্রকে বজায় রাখার স্বাধীনতা, যা খুশি লেখার স্বাধীনতা, এবং এই স্বাধীনতা নামের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠলে সব সংবাদপত্র মালিকদের সংগঠিতভাবে আঘাত হানার স্বাধীনতা।
O
সম্পাদক থেকে সাংবাদিকরা মালিকের কাছে ‘পেপার পলিসি’ মেনে লেখার ও তা প্রকাশ করার অলিখিত চুক্তির বিনিময়েই চাকরিতে ঢোকেন। পেপার পলিসিকে অমান্য করার মত ধৃষ্টতা কেউ দেখালে, পরের দিনই তার স্থান হবে পত্রিকা অফিসের পরিবর্তে রাস্তায়।
এইসব পত্রিকাগুলোর সম্পাদক থেকে সাংবাদিকদের অবস্থান মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহামেডানের ফুটবল টিমের কোচ ও খেলোয়াড়দের মতই—যখন যে দলে খেলবেন, সেই দলকে জয়ী করতেই সচেষ্ট থাকেন। প্রতিক্রিয়াশীল পত্রিকা বলে যাকে আপনি গাল পাড়েন, তারই অতিক্ষমতা সম্পন্ন দুঁদে বার্তাসম্পাদক কিংবা ঝাণ্টু সাংবাদিক আপনার মনে হওয়া প্রগতিবাদী পত্রিকায় যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবিকার স্বার্থে কলম থেকে ঝরাতে থাকেন বিপ্লবী আগুন। একইভাবে বিপরীত ঘটনাও ক্রিয়াশীল। প্রগতিশীল পত্রিকার বিপ্লবী কলমও টিম পাটাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবিপ্লবী কলম হয়ে ওঠে। এই জাতীয় উদাহরণ কিন্তু ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত নয়, বরং সাবলীল গতিশীল। এইসব বিপ্লবী, প্রতিবাদ, প্রতিবিপ্লবী, বুর্জোয়া প্রভৃতি প্রতিটি বাণিজ্যিক পত্রিকার মালিকদের মধ্যে অবশ্যই প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে। একজনকে ধন-সম্পদে আর একজনের টপকে যাওয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কিন্তু সামগ্রিকভাবে নিজেদের অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক কোনও শক্তির বিরুদ্ধে মোকাবিলার ক্ষেত্রে বা দারুণ! রকম এককাট্টা।
সংবাদপত্রগুলোর ভানের মুখোশটুকু সরালে দেখতে পাবেন, প্রতিটি সংবাদপত্রই বর্তমান সমাজ কাঠামোর স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষে জনমতকে পরিচালিত করে এবং বহিরঙ্গে এরা সরকার -পুলিশ-প্রশাসনের কিছু কিছু দুর্নীতির কথা ছেপে সিস্টেমকে টিকিয়ে রাখার মূল ঝোঁককে আড়াল করে। এমন সব দুর্নীতির কথা পাবলিক খায়’ বলেই পত্রিকাগুলো ছাপে। এই সমাজ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার চাবিকাঠি যাদের হাতে, তারা জানে, এমন দু-চারটে দুর্নীতি ধরার লালিপপ্ হাতে ধরিয়ে দিয়ে কীভাবে অত্যাচারিতের ক্ষোভের আগুনে জল ঢালতে হয়। তারা জানে, সিস্টেমের প্রেসার কুকারে নিপীড়িতদের ফুটন্ত ক্ষোভকে বের করে দেওয়ার ‘সেফটি ভালভ’ হলো মাঝে-মধ্যে দু-চার জনের দুর্নীতি ফাঁস। পরে অবশ্য শাস্তি-টাস্তি না দিলেও ক্ষতি নেই। জনগণের স্মৃতি খুবই দুর্বল। ভুলে যাবে প্রতিটি ঘটনা, যেভাবে ভুলেছে বফর্স কেলেংকারি, শেয়ার কেলেংকারি। আর এর ফলে একআধটা রাজনৈতিক নেতা, পুলিশ বা প্রশাসক যদি বধ হয়, তাতেও অবস্থা একটুও পাল্টাবে না। ফাঁকা জায়গা কোনও দিনই ফাঁকা থাকে না, থাকবে না। এক যায়, আর এক উঠে আসে।
গত কয়েক বছরে আমরা বিভিন্ন ধরনের দাবি আদায়ের আন্দোলন গড়ে উঠতে দেখেছি। ‘চিপকো’, ‘নর্মদা বাঁচাও’-এর মত বিভিন্ন দাবি বা ইস্যু-ভিত্তিক আন্দোলনের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা আমাদের আছে। আমরা মনে করি, এইসব আন্দোলনের সামাজিক প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু এইসব আন্দোলন যেহেতু অসাম্যের সমাজ কাঠামো বা ‘সিস্টেম’ পাল্টে দেওয়ার লক্ষ্যে পরিচালিত নয়, তাই সমাজ কাঠামো জিইয়ে রাখার অংশীদার রাজনৈতিক দল, প্রচারমাধ্যম, বুদ্ধিজীবী ইত্যাদিরা দলগত-স্বার্থ, ব্যক্তিগত স্বার্থ, ব্যক্তি ইমেজ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে অনেক অঙ্ক কষে এই জাতীয় আন্দোলনকে সমর্থন বা অসমর্থন করেন।
এই বক্তব্যকে স্পষ্টতর করতে উদাহরণ হাজির করাটা বোধহয় বাহুল্য হবে না। দৃষ্টান্ত হিসেবে ‘নর্মদা বাঁচাও’ আন্দোলনকেই না হয় বেছে নেওয়া যাক। ‘নর্মদা বাঁচাও’ আন্দোলন কিসের আন্দোলন, আসুন একটু বুঝে নেওয়া যাক। নর্মদা নদীর উপর সর্দার সরোবর প্রকল্পে বাঁধ দিয়ে জল সঞ্চয় করতে গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের যে চল্লিশ হাজার পরিবার বাস্তুচ্যুত হবে, সুদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে তিন রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু এখনও প্রতিশ্রুতি পালন করেনি। এখন পর্যন্ত মাত্র ছ হাজার পাঁচশো বাস্তুচ্যুত পরিবারের জন্য জমি বিলি হয়েছে। প্রতিটি বাস্তুচ্যুত পরিবারের পুনর্বাসনের লক্ষ্যকে কেন্দ্রবিন্দু করে গড়ে উঠেছে ‘নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন’। কোনও সন্দেহ নেই, এই আন্দোলন চৌতিরিশ হাজার পাঁচশো পরিবারের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয় এক আন্দোলন| এই আন্দোলনের প্রতি আমাদের সমিতির আন্তরিক সমর্থন রয়েছে। তারপরও একটা প্রয়োজনীয় প্রশ্ন উঠে আসতে পারে। এই আন্দোলন যদি লক্ষ্য পূরণে সমর্থ হয়, অর্থাৎ তিন রাজ্যের সরকার যদি বাঁধ তৈরির জনা বাস্তুহারা প্রতিটি পরিবারকে জমি বিলি করে, তারপরে কীহবে? উত্তর একটাই। জয়ের মধ্য দিয়ে ‘নর্মদা বাঁচাও নান্দোলন’-এর পরিসমাপ্তি ঘটবে। আমাদের দেশের অসাম্যের সমাজ কাঠামোয় একটিও আঁচ না কেটেই পরিসমাপ্তি ঘটবে।
‘ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি’ যে সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সামিল হয়েছে, সে আন্দোলনের লক্ষ্য-অসাম্যের সমাজ কাঠামো ভেঙে সাম্যের সমাজ কাঠামো গড়ে তোলা। এবং তারপরও সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে গতিশীল রাখা। কারণ, ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান থেকে আমরা এই শিক্ষা নিয়েছি যে, সাম্যের সমাজ কাঠামো গড়ে উঠলেও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রয়োজন শেষ হয়ে যায় না। অসাম্যের ঘুণ পোকার আক্রমণ থেকে মানুষের চেতনাকে বাঁচাতে, সাম্যের সমাজ কাঠামোকে বাঁচাতে সাংস্কৃতিক আন্দোলন বিকল্পহীন।
আমাদের সমিতি বিভিন্ন ইস্যু ভিত্তিক আন্দোলনে বার বার সামিল হয়েছে। আন্দোলন কখনও জ্যোতিষী বা ধর্মগুরুদের ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে; কখনও বা ভারতীয় সংবিধানে দেওয়া ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যাকে পূর্ণ-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করতে রাষ্ট্রীয় পদাধিকারীদের ‘বিশ্ব ধর্ম সম্মেলন’-এ অংশগ্রহণ থেকে বিরত করতে; আবার কখনও বা ড্রাগ অ্যাণ্ড ম্যাজিক রেমেডিস (অবজেকশন্যাবল অ্যাডভারটাইজমেণ্ট অ্যাক্ট, ১৯৫৪-কে আইনের বইয়ের পাতা থেকে তুলে এনে প্রয়োগ করতে। প্রতিটি ইস্যু ভিত্তিক আন্দোলনেই একের পর এক জয় আমরা এনেছি। কিন্তু কোনও জয়ের মধ্য দিয়েই আমাদের সমিতির আন্দোলনের প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়নি। এমনকি অসাম্যের সমাজ কাঠামোকে চূড়ান্ত আঘাতে ভেঙে ফেলার পরও আমাদের এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রয়োজন হারিয়ে যাবে না। সাম্যের সমাজ কাঠামো গড়ে তোলার পরও নয়। কারণ যুক্তিবাদী আন্দোলন বা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অভাবে ক্ষমতার ঘুণপোকা, ৰীতির ঘুণ পোকা সাম্যের সমাজ কাঠামোকে কুরে কুরে ফোঁপরা করে দেবে।
‘নর্মদা বাঁচাও…’এর মত এইসব দাবি আদায়ের আন্দোলন সমাজ কাঠামো বা সিস্টেম পাল্টে দেওয়ার লক্ষ্যে পরিচালিত নয়, তাই এই জাতীয় আন্দোলন সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমর্থন যেমন অনেক সময়ই পেয়ে ঋকে, তেমনই প্রচার মাধাম্যগুলো নিজেদের প্রগতিশীল ইমেজ তৈরি করতে এদের প্রচার দেয়।
যদিও কোনও বাণিজ্যিক পত্রিকা দিব্যি গেলে নিজেদের যুক্তিকামী ও সামাকামী দল ঘোষণা করেন, তাহলে তখনাৎ তা মন্ত্রী বা মাতালের ‘ভাট-বকা’ বলে ধরে নিয়ে বাতিল করতে পারেন। কারণ, এটাই পরম সত্য যে-পত্রিকায় পুঁজি নিয়োগ করা কোটিপতি ব্যবসায়ী কখনই চাইবেন না, যুক্তির পথ ধরে সাম্যের সমাজ গড়ে হক, আর তিনি ধনকুবের থেকে সাধারণ মানুষের আর্থিক মানে নেমে আসুন। তাই এঁরা সঠিক সাম্যের আন্দোলনকে ঠেকাতে যড়যন্ত্রের সমস্ত রকম ফাঁদ পাতার শাসনতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষিত রাখেন ও প্রয়োগ করেন। একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ নমুনা হিসেবে আপনাদের সামনে পেশ করছি। পাঠক-পাঠিকাদের কাছে যুক্তিবাদের প্রচারক বলে পরিচিত একটি বাংলা দৈনিক পত্রিকার স্ববিরোধী আচরণ, যা যুক্তিবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ ও সাম্যবাদের পক্ষে মননের বিকাশকামী গ্রন্থসমূহের প্রকাশ ও প্রচারকে ঠেকাতে পত্রিকাটি মুখোশের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো। সম্পাদক তাঁর কলমে (২৪ সেপ্টেম্বর ‘৯৫) এ’জাতীয় কেতাব’ বছর বছর প্রকাশের প্রতি তীব্র শ্লেষ ও বিদ্রুপের বিষ ছুঁড়ে দিলেন। আর তারপরই কিছু কিছু বিপ্লবী-বুদ্ধিজীবী, পত্রিকা-সম্পাদকের সন্তোষ উৎপাদনই নিজেকে আলোকিত করার সহজ উপায় বিবেচনায়, সম্পাদকের সুরে সুর মিলিয়ে যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদের বই-পত্তর প্রকাশের বিরুদ্ধে বিষ উগড়ে দিতে শুরু করেছেন। এমনও হতে পারে, বুদ্ধিজীবীদের এমন অদ্ভুত আচরণের পিছনে রয়েছে সম্পাদকের সুস্পষ্ট নির্দেশ। বুদ্ধিজীবীদের স্পনসরকারী পত্রিকাগুলো মাঝে-মধ্যে বুদ্ধিজীবীদের নির্দেশ দেন একথা তো বাস্তব সত্য।
প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, আপনি আমি আমরা যখন চাইছি হাজার-হাজার বছরধরে ভাববাদী চিন্তার লক্ষ-কোটি বই যেভাবে মানুষকে অন্ধকারের মধ্যে, অসাম্যের শিকলে বন্দি করে রেখেছে, সেই শিকল ভেঙে মুক্তির স্বাদ দিতে যুক্তি-প্রসারী বই বেরিয়ে আসুক প্রতিটি দিনে, প্রতিটি মুহূর্তে, ঠিক সেই সময় যুক্তিবাদের নিধন লিপ্সায় মত্ত ঘাতকেরা কাদের দালালি করছে? বাঁচার জন্যেই প্রয়োজন এঁদের চিনে নেওয়ার, এঁদের চিনিয়ে দেওয়ার, এঁদের প্রতি ঘৃণা ছুঁড়ে দেওয়ার।
কুসংস্কার বিরোধী, ভাববাদ বিরোধী লেখা প্রকাশের মধ্যে জ্ঞানবাবারা অর্থ রোজগারের ধান্ধাও খুঁজে পান, এবং সে প্রসঙ্গ তোলেন-ও। রবীন্দ্রনাথ থেকে সত্যজিৎ, বড়ে গোলাম আলি থেকে আমজাদ আলির সৃষ্টির ক্ষেত্রে কেন বাণিজ্যের গন্ধ পাওয়ার প্রসঙ্গ তোলেন না? জেম্স্ র্যাণ্ডি থেকে কভুরের বুজরুকি ফাঁসের লেখাতে কেন অর্থের আঁশটে গন্ধ পান না? দেবীপ্রসাদ থেকে আজিজুল হকের লেখাকে বাতিল করতে কেন অর্থ মূল্যকে যুক্ত করেন না? যুক্তিযুক্ত নয় বরং আহাম্মকী বলেই কী? এরা গণচেতনা বাড়াবার জন্য গাঁটের কড়ি দিয়ে বই ছাপিয়ে, বিনামূল্যে বিলিয়েছেন বলে তো শুনিনি! তাহলে কোন যুক্তিতে যুক্তিবাদী, মানবতাবাদী এবং সাম্যবাদী মননের বিকাশকামী গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে এই হাস্যকর অভিযোগের কাদা ছোঁড়া? শুধুমাত্র কাদা ছোঁড়ার পরিকল্পনাকে সার্থক করে তুলতেই কী?
O
কুসংস্কার বিরোধী, ভাববাদ বিরোধী লেখা প্রকাশের মধ্যে জ্ঞানবাবারা অর্থ রোজগারের ধান্ধাও খুঁজে পান, এবং সে প্রসঙ্গ তোলেন-ও। রবীন্দ্রনাথ থেকে সত্যজিৎ, বড়ে গোলাম আলি থেকে আমজাদ আলির সৃষ্টির ক্ষেত্রে কেন বাণিজ্যের গন্ধ পাওয়ার প্রসঙ্গ তোলেন না? জেম্স্র্যাণ্ডি থেকে কভুরের বুজরুকি ফাঁসের লেখাতে কেন অর্থের আঁশটে গন্ধ পান না? দেবীপ্রসাদ থেকে আজিজুল হকের লেখাকে বাতিল করতে কেন অর্থ মূল্যকে যুক্ত করেন না?
O
যাঁরা বেছে বেছে শুধুমাত্র যুক্তিবাদের পক্ষে, বুজরুকি ফাঁসের পক্ষে লেখা বই-পত্তরের ক্ষেত্রে লেখকের বাণিজ্যিক মানসিকতার গন্ধ পান, তাঁদের কিন্তু আদৌ অজানা নয়, বুজরুকি ফাঁসে বিরত থাকলে রোজগারটা লেখক অকল্পনীয় অংকে নিয়ে যেতে পারেন। আজ থেকে বছর দশেক আগে ফিলিপিনের ফেইথ হিলারের রহস্যকে উন্মোচন না করার জনা পনের লক্ষ টাকার ভেট দিতে বাড়ি এসে ধনকুবেরের তোয়াজ করে যাওয়ার কাহিনী সেই কবে ‘অলৌকিক নয়, লৌকিক’ এর দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তৃত ভাবে লেখা হয়েছে। দশ বছর আগের পনের লক্ষ টাকা এখনকার কোটি টাকার সমান কি না, সে কূট প্রশ্নে না গিয়েও বলি—এটি একটিমাত্র উদাহরণ, সব নয়। পরিবর্তে আমরা কি দেখেছি? বিকল্প চিকিৎসা নিয়ে কলকাতা দূরদর্শনের নিউজ ম্যাগাজিনের জন্য একটি ছবি তুলেছে একটি প্রাইভেট কোম্পানী। ছবিটিতে যুক্তিবাদী সমিতির পক্ষে হাজির করা কলকাতার বিশিষ্ট চিকিৎসকদের নানা প্রশ্নের মুখে বিকল্প চিকিৎসকরা হাসির খোরাক হলেন। বিকল্প চিকিৎসকদের এক একজনের জ্ঞানের পরিধি বাস্তবিকই হাস্যকর ছিল। প্রযোজক ছবিটি দেখাবার দিন-ক্ষণও ঘোষণা করলেন। সেদিন ছবি দেখতে গিয়ে দর্শকরা বোকা বনলেন! স্বর্ণসন্ধানী ব্যবসায়ীর কাছে বোকা বনলেন: কারণ ছবিটি দেখান হয়নি। অন্য একটি অনুষ্ঠান জায়গা দখল করেছিল। এবং স্পনসরের ভূমিকায় দেখতে পাওয়া গেল একটি বিকল্প চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত সংস্থাকে। অনেক চেঁচামেচিতে পরের সপ্তাহে ছবিটি যদিও বা এলো, তবে তখন পরিকল্পিত কাঁচি চালনার কল্যাণে সত্য হয়েছে বিকৃত এবং বিকল্প চিকিৎসা ‘বিজ্ঞান-টিজ্ঞান’, এবং স্পনসরের ভূমিকায় আবারও প্রবলভাবে হাজির হলো বিকল্প চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত সংস্থাটি।
প্রচারে ভারত বিখ্যাত মহারাষ্ট্রের এক ম্যাগনেটোথেরাপিস্ট কলকাতায় ক্যাম্প করেছিলেন কয়েকদিনের। ব্যবস্থাপত্র মিলছিল বিনি পয়সায়। চুম্বক চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম কিনতে হচ্ছিল, এবং তা স্বপ্ন-মূল্যেই। প্রতিদিনের আয়টা স্বভাবতই ছিল কল্পনাতীত। ম্যাগনেটো-থেরাপিস্টের ডাক্তারী ডিগ্রিটা এক অস্তিত্বহীন বিশ্ববিদ্যালয়ের। একটি বাংলা দৈনিকের পক্ষে সত্যানুসন্ধানে নেমেছিলাম। লেখায় হাজির করলাম ওঁর বুজরুকি ও বে-আইনি ব্যাপার-স্যাপার। লেখা শেষ হয়েছিল সরাসরি চলেঞ্জ জানিয়ে। তারপর কোথা থেকে কি হল—লেখাটি আজও প্রকাশের মুখ দেখেনি। পরিবর্তে শুনতে হয়েছে চুম্বক চিকিৎসা ক্যাম্পের এক ব্যবস্থাপকের বিদ্রুপ—লেখাটা পারলেন ছাপাতে?
এক ধনবান জাদুকরের একটি বিখ্যাত প্রতারণার খুঁটি-নাটি তথ্য-প্রমাণ আমাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে কিছু সাংবাদিক যতটা সচেষ্ট হয়েছিলেন, প্রমাণগুলো পেতেই ততটাই নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়েছিলেন, কোনও এক গভীর গোপন কারণে।
শুধু একটা-আধটা খবর চেপে দেওয়ার বিনিময়ে ‘আলতু-ফালতু’দের অনেকেই যখন শান্তিনিকেতনে বাড়ি, কলকাতায় সাজান ফ্লাট, ঝাঁ-চকচকে দোকান কামিয়েছেন, তখন এই লেখক না লেখার বাজার দর কোথায় তুলতে পারতেন, চিরকালের জন্য মুখ বন্ধ রাখার ‘মুখ মাঙ্গে’ দরটা কোথায় নিয়ে যেতে পারতেন—এটা একটু অনুমান করার চেষ্টা করুন প্রিয় পাঠক-পাঠিকা।
ভারত তথা পৃথিবীর ইতিহাসে আধুনিক যুক্তিবাদের যে বীজাঙ্কুর রোপিত হয়েছিল ভারত ভুমিতে, দশ বছরে তার শিকড় দ্রুত ছড়িয়েছে দেশ ও প্রতিবেশী দেশের শিরা শিরায়। যে সমাজ উত্তরণের পথে, সেখানে থাকে শ্রেণীদ্বন্দ্ব, শ্রেণীসংগ্রাম। যুক্তিবাদের পথ ধরে সাম্যের সমাজ গড়ার লক্ষ্যে এগুতে আমাদের সমাজ আজ অনিবার্য শ্রেণীদ্বন্দ্ব বা শ্রেণীসংগ্রামের মুখোমুখি। যুক্তিবাদের এই প্রবল সম্ভাবনাময় উখানে সন্ত্রস্ত অসাম্যের সমাজ কাঠামোর নিয়ন্তা ধনকুবের গোষ্ঠী ও তাদের সহায়ক শক্তিগুলো। আর তারই পরিণতিতে আমজনতার সাংস্কৃতিক মগজ ধোলাইয়ের জন্য নামন হয়েছে রাষ্ট্রশক্তি, নির্বাচন নির্ভর আখের গোছান রাজনৈতিক দল, প্রচার মাধ্যম, ভাড়াটে বুদ্ধিজীবী, প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহ এবং ধর্মীয় শিবিরকে। ওরা সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সাংস্কৃতিক মগজ ধোলাইয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে ময়দানে নেমেছে। পালন করে চলেছে নিজ নিজ কর্তব্য।
প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন, যুক্তিবাদী আন্দোলনকে বিভাজিত করতে ও কালিমালিপ্ত করতে বিরোধ যাদের মূলধন, সেইসব যুক্তিবাদী আন্দোলনের স্বঘোষিত অভিভাবক ও প্রচার মাধ্যমের মুখেই অহরহ ঐক্যের বাণী। ওদের এই স্ববিরোধিতাকে ভণ্ডামি বলে উড়িয়ে দিলে ভুল হবে। কারণ ওদের এমন ভণ্ডামির পিছনে যে উদ্দেশ্য রয়েছে তা আরও অনেক বেশি বিপজ্জনক। ওদের কাছে ‘ঐক্য’ মানে একটা ছাঁচ। মানুষের অন্ধ বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তির সহাবস্থানের একটা ছাঁচ। না-যুক্তিবাদীদের সঙ্গে, ‘যুক্তিবাদী’দের সহাবস্থানের একটা ছাঁচ।
যারা এই ছাঁচে নিজেদের ঢালতে রাজি নয়, লক্ষ্যে পৌঁছতে তাদের সামনে পড়ে আছে দীর্ঘ সংগ্রামের পথ। কাজটি কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ হলেও অসম্ভব নয়।
সুন্দর সমাজ গড়ার স্বার্থে কাঁটার মুকুট মাথায় পরেই আসুন আমরা সংঘর্ষে নামি। নির্মাণকাজের আগে প্রয়োজনীয় সংঘর্ষে।