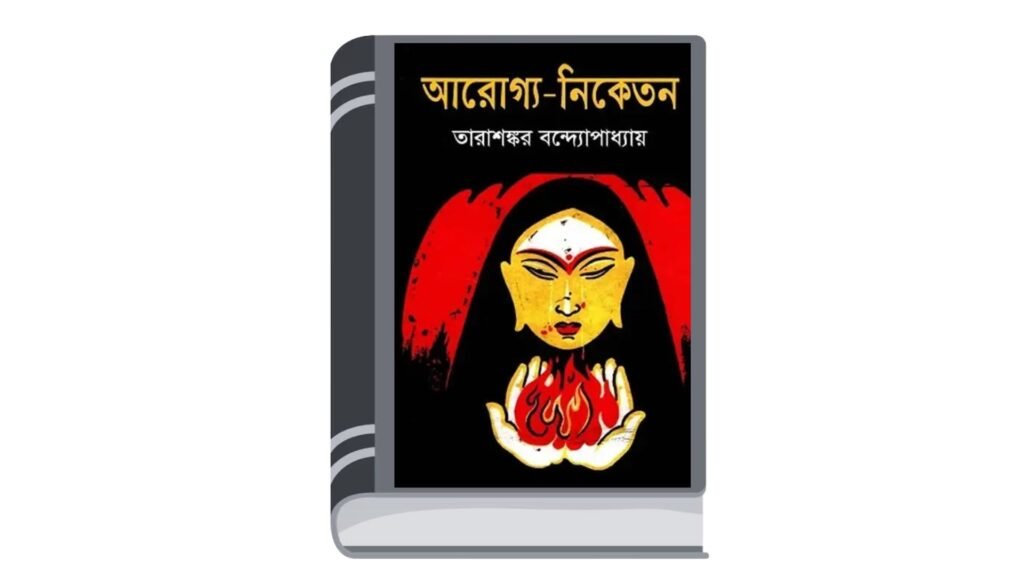০৩. জীর্ণ আরোগ্য-নিকেতনের দাওয়ায়
জীর্ণ আরোগ্য-নিকেতনের দাওয়ায় তখন জনদশেক রোগী এসে বসে আছে। এদের অধিকাংশই মুসলমান। আজ তিন পুরুষ ধরে দীনবন্ধু মশায়ের আমল থেকে মশায় বংশ পুরুষানুক্রমে চিকিৎসাই করে আসছেন। জীবন মশায় আজ বৃদ্ধ, আসক্তিহীন, উৎসাহহীন কিন্তু তবু এরা তাকে ছাড়ে না। একমাত্র পুত্র মারা গেছে, নতুন কালের চিকিৎসাবিজ্ঞান এসেছে তার বিপুল সমারোহ নিয়ে, নিজে স্থবির হয়েছেন, সংসারে শান্তি নাই, জীবন মশায় মধ্যে মধ্যে ভাবেন। একেবারেই ছেড়ে দেবেন। কিন্তু দেব-দেব করেও দিতে পারেন না, দেওয়া হয় না। আজ তিনি ভাবলেন না। আর না, আজই শেষ করবেন।
আরোগ্য-নিকেতনে আজ আর ওষুধই নাই; ও ব্যবস্থা ডাক্তার উঠিয়ে দিয়েছেন। আজকাল প্রেসক্রিপশন লিখে দেন। নবগ্রাম বি কে মেডিক্যাল স্টোর্স ওষুধ দেয়। দু-তিন মাস অন্তর কিছু অর্থও দেয় কমিশন বাবদ।
এখনও ওই ভাঙা আলমারি তিনটের মাথায় ওষুধের হিসেবের খাতা স্থূপীকৃত হয়ে জমা হয়ে রয়েছে। খেরো-মলাটগুলো আরশোলায় কেটেছে। ভিতরের পাতাগুলি পোকায় কেটে চালুনির মত শতছিদ্র করে তুলেছে। তবু আছে। ডাক্তারের দুর্ভাগ্য উই নেই; অথবা কোনোদিন অগ্নিকাণ্ড হয় নি। জঞ্জাল হয়ে জমে আছে। ওগুলোর দিকে তাকিয়ে জীবন দত্ত হাসেন। ওর মধ্যে অন্তত বিশ-ত্রিশ হাজার টাকা পাওনার হিসেব আছে। বেশি, আরও বেশি। তিন পুরুষের হিসেব ধরলে লক্ষ টাকা। তাঁর আমলের—তাঁর নিজের পাওনা অন্তত ওই বিশ হাজার টাকা।
পিতামহ দীনবন্ধু দত্ত নবগ্রামে রায়চৌধুরী বংশের আশ্রয়ে এসে পাঠশালা খুলেছিলেন, পাঠশালা করতেন, রায়চৌধুরীদের দেবোত্তরের খাতা লিখতেন, কিছু আদায় করতেন। ওই রায়চৌধুরীদের বাড়িতে চিকিৎসা করতে আসতেন কবিরাজ-শিরোমণি কৃষ্ণদাস সেন। দীনবন্ধু দত্তকে তিনিই শিষ্যত্বে গ্রহণ করেছিলেন। রায়চৌধুরী বংশের বড়তরফের কর্তার একমাত্র পুত্রের সান্নিপাতিক জ্বরবিকার হয়েছিল; জীবনের আশা কেউই করে নি; মা শয্যা পেতেছিলেন, বাপ। স্থাণুর মত বসে থাকতেন, তরুণী পত্নীর চোখের জলে নদীগঙ্গা বয়ে যাচ্ছিল। আশা ছাড়েন নি শুধু ওই কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়। তিনি বলেছিলেন একজন ধীর অক্লান্তকর্মা লোক চাই, সেবা করবে। তা হলে আমি বলতে পারি, রোগের ভোগ দীর্ঘ হলেও রোগী উঠে বসবে। সেবা করতে এগিয়ে এসেছিলেন দীনবন্ধু দত্ত। দীর্ঘ আটচল্লিশ দিনের দিন জ্বর ত্যাগ হয়েছিল। কবিরাজ দীনবন্ধুকে বলেছিলেন-আজও তোমার ছুটি হল না। অন্তত আরও চব্বিশ দিন তোমাকে সেবা করতে হবে। এই সময়টাতেই সেবা কঠিন। এখন স্নেহান্ধ আত্মীয়স্বজনেরা স্নেহাতিশয্যে সেবার নামে রোগীর অনিষ্ট করবে। রোগীকে কথা বলাবে বেশি, কুপথ্যও দেবে। এই সময়ে তোমাকে বেশি সাবধান হতে হবে। তাও দীনবন্ধু নিখুঁতভাবে করেছিলেন।
সন্তান আরোগ্য লাভ করাতে বড়কর্তা দীনবন্ধু দত্তকে পুরস্কৃত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দীনবন্ধু তা গ্রহণ করেন নি। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছিলেন আমি তোমাকে পুরস্কার দেব। প্রত্যাখ্যান কোরো না। ধীরতা তোমার আশ্চর্য, বুদ্ধিও তোমার স্থির; লোভেও তুমি নির্লোভ। তুমি চিকিৎসাবিদ্যা শেখ আমার কাছে। তুমি পারবে।
চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করে নবগ্রামের পাশে এই ছোট শান্ত গ্রামখানিতে তিনি বাস। করেছিলেন। নবগ্রামে বাস করেন নি। গ্রামখানি ব্রাহ্মণ জমিদার বংশ-অধ্যুষিত, সুতরাং সেখানে কলহ অনেক এবং সেখানে বাজার আছে কাছেই, তাই কোলাহলও বড় বেশি। এসব থেকে দূরেই তিনি থাকতে চেয়েছিলেন। বলতেন—দেবতারা প্রসন্ন সহজে হন না, কিন্তু রুষ্ট হন এক মুহূর্তে; সামান্য অপরাধে আজীবন সেবার কথা ভুলে যান। আর বাজারে থাকে বণিক। সেখানে চিন্তার অবকাশ কোথা?
মশায় উপাধি পেয়েছিলেন এই দীনবন্ধু মশায়ই। পরনে থান-ধুতি, পায়ে চটি, খালি গা, দীনবন্ধু মশায় গ্রামান্তরে রোগী দেখে বেড়াতেন। এ অঞ্চলে প্রতিটি বালক তাঁকে চিনত। তিনি ডেকে তাদের চিকিৎসা করতেন; মধু খাওয়াতেন। টিনবন্দি মধু থাকত। আর আশ্চর্য ছিল তার সাধুপ্রীতি। সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ করে, তাদের পরিচর্যা করে বহু বিচিত্র মুষ্টিযোগ তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। ভণ্ড সন্ন্যাসীর কাছে ঠকেছেনও অনেক। তাতে তার আক্ষেপ বা অনুশোচনা ছিল না; কিন্তু এ নিয়ে কেউ তাকে নির্বোধ বলে রহস্য বা তিরস্কার করলে বলতেন—সেই আমাকে ঠকিয়েছে, আমি তো তাকে ঠকাই নি। আমার আক্ষেপ কি অনুতাপের তো হেতু নাই। শুধু কি সন্ন্যাসীকত বেদে, ওস্তাদ, গুণীন—এদের কাছেও তাদের বিদ্যা তিনি সংগ্রহ করেছিলেন।
পুত্র জগদ্বন্ধু দত্ত ছিলেন উপযুক্ত সন্তান। তিনি পিতার কাছে সমস্ত বিদ্যাই আয়ত্ত করেছিলেন। মৃত্যুকালে দীনবন্ধু মশায় ছেলেকে বলেছিলেন বিষয় কিছু পারি নি করতে কিন্তু আশয় দিয়ে গেলাম মহৎ। মহাশয়ত্বকে রক্ষা কোরো। ওতেই ইহলোক পুরলোক দুই-ই সাৰ্থক হবে।
জগদ্বন্ধু দত্ত পিতৃবাক্য অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ করেছিলেন। তাকেও লোকে বলত—জগৎ মশাই। পিতার অর্জন করা মহাশয়ত্ব তিনি রক্ষাই করেন নি, তাকে উজ্জ্বলতর করেছিলেন। তিনি রীতিমত সংস্কৃত শিখে আয়ুর্বেদ পড়েছিলেন। পারুলিয়ার বৈদ্যপাটের ছাত্র তিনি চিকিৎসক হিসেবে আয়ুর্বেদশাস্ত্রে যেমন ছিল ব্যুৎপত্তি তেমনি ছিলেন নির্লোভ এবং রোগীর প্রতি স্নেহপরায়ণ। আবার মানুষ হিসেবে যেমন ছিল তার মর্যাদাবোধ তেমনি ছিল প্রকৃতির মধুরতা। সে মধুরতা প্রকাশ পেত তার মিষ্ট ভাষায়, সূক্ষ্ম রসবোধে ও রসিকতায়। তাঁর রসিকতার কয়েকটি স্মৃতি এখানকার মানুষের রসশাস্ত্রের অলিখিত ইতিকথায় কয়েকটি অধ্যায় হয়ে আছে। তাঁর রসিকতার সবচেয়ে বড় কথা এই যে, তাতে কটু বা অম্লরসের একটুকু প্রক্ষেপ থাকত না। মানুষকে মধুর রসে আপ্লুত করে দিত। প্ৰসন্ন হয়ে উঠত রসিকতায় অভিষিক্ত জনটি।
এই যে লাল কাঁকরের পাকা রাস্তাটি নবগ্রাম থেকে এই গ্রামে এসে পৌঁছেছে এবং এই গ্রাম পার হয়ে উত্তর দিকে বিস্তীর্ণ মাঠখানির বুক চিরে চলে গিয়েছে—ওই রাস্তাটির কথা উঠলেই লোকের মনে পড়ে যায় জগত্মশায়ের কথা, তার রসজ্ঞানের কথা এবং সঙ্গে সঙ্গে মন সরস ও প্রসন্ন হয়ে ওঠে। আপন মনে একা একাই লোকেরা হেসে সারা হয়।
পঁয়তাল্লিশ বৎসর আগে। তখন এখনকার এই পরিচ্ছন্ন গ্রাম্য সড়কটির শুধু আকারই ছিল, আয়তনও একটা ছিল, অবয়বও ছিল, কিন্তু কোনো গঠনই ছিল না। একটা অসমান, খানাখন্দে বন্ধুর এবং দুর্গম গো-পথ ছিল। বর্ষার সময় এক-বুক কাদা হত। সে কাদা একালে কেউ কল্পনাই করতে পারবেন না। মশায়ের রসিকতার কাহিনীটি থেকেই তা বুঝতে পারবেন।
এখনও দেবীপুরে সেকালের খানাখন্দের নাম শুনতে পাওয়া যায়। একটু প্রবীণ দেখে যাকে খুশি জিজ্ঞাসা করবেন—সে নাম বলবে—চোরধরির গাদ অর্থাৎ কাদা; মানে যে কাদায় পড়ে। চোর ধরা পড়ে যায়। গরুমারির খাল-ও খালটায় চোরাবালির মত একটা চোরা গর্তে ব্ৰজ পরামানিকের একটা বুড়ি গাই পড়ে মরেছিল। এই কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ হেসে উঠবে। না হেসে থাকে কী করে? ভাবুন তো ব্যাপারটা! ব্ৰজর গরু মরল, কিন্তু সে বিপদের চেয়েও বড় বিপদ হল—ব্রজ যে প্ৰায়শ্চিত্ত করবে তার মাথা কামাবে কে? সে নিজে নাপিত, ক্ষুর তার আছে, কিন্তু চালাবে কে? এখনকার মত তখন তো সবাই ক্ষুর চালাতে জানত না। জানলেও নিজের হাতে মাথা কামানো নিশ্চয় যায় না। শেষে ওই জগদ্বন্ধু মশায়ই দিয়েছিলেন ব্রজর মাথা কামিয়ে। কবিরাজ ছিলেন, বিকারগ্রস্ত রোগীর মাথা অনেক সময় তাঁকে কামিয়ে দিতে হত। কি না। এসব রোগীর মাথায় ক্ষুরের মত অস্ত্র চালাতে তিনি পরামানিকের হাতে ক্ষুর ছেড়ে দিতেন না। সেদিন ব্ৰজর মাথা কামাতে বসে তার মাথাটি বাঁ হাতে ধরে নিজেই হেসে ফেলেছিলেন, কামাবার সময় জগদ্বন্ধু মশায় হেসেই বলেছিলেন, ব্ৰজ, আজ শোধ নিই?
-আজ্ঞে? ব্ৰজ অবাক হয়ে গিয়েছিল—শোধ? কিসের শোধ?
—কামাবার সময় অনেক রক্ত দেখেছ বাবা, আজ আমি দেখি? শোধ নিই?
এই রাস্তাকে ভাল করেছেন তিনি অর্থাৎ জীবন মশায় নিজে। তিনিই ওই কাঠের নামফলকখানা টাঙিয়েছিলেন। জগদ্বন্ধু মশায় ছিলেন কবিরাজ। জীবন মশায়ডাক্তার কবিরাজ দুই। তখনকার দিনে একটা কথার চলন ছিল ঘরে ঘরে। জগৎ খাবি, না জীবন খাবি? সেকালে অসুখ হলে বাড়ির লোক রোগীকে প্রশ্ন করত জগৎ খাবি, না জীবন খাবি? অর্থাৎ ডাক্তারি ওষুধ খাবি-জীবন দত্তকে ডাকব? না-কবিরাজি ওষুধ খাবি-জগদ্বন্ধু কবিরাজ মশায়কে ডাকব?
যাক। আজ ওই কথাটা চিরদিনের মত ভুলে যাক লোকে।
—মশায়! বাবা!
জীবন মশায় আহত অন্তর নিয়ে ফিরে এসে ডাক্তারখানায় স্তব্ধ হয়ে বসলেন, স্থির নিম্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন বাইরের দিকে। আজ থেকে শেষ। শেষ হয়ে যাক মশার বংশের মশায় উপাধি চিকিৎসকের কাজ। যাক।
এরই মধ্যে শেখপাড়ার বৃদ্ধ মকবুল এসে দরজার মুখে বসে তাকে ডাকলে—মশায়! বাবা!
একটা দীর্ঘনিশ্বাস আপনাআপনি বেরিয়ে এল জীবন মশায়ের বুক থেকে।–কে? তিনি সচেতন হয়ে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন মকবুলের দিকে।
মকবুল বললেহাতটা একবার দেখেন বাবা। বড় কষ্ট পাচ্ছি এই বুড়া বয়সে। অষ্টাঙ্গে দরদ। ঘুষঘুষা জ্বর। মাটি নিতে হবে তা আমার মালুমে এসেছে। কিন্তু এই কষ্ট—এ যে সইতে নারছি বাবা। ইয়ার একটা বিধান দ্যান।
মশায় ঘাড় নেড়ে বললেন–আমার কাছে তোমরা আর এসো না মকবুল। চিকিৎসা আর আমি করব না। একালে অনেক ভাল চিকিৎসা উঠেছে, হাসপাতাল হয়েছে, নতুন ডাক্তার এসেছে। তোমরা সেইখানেই যাও।
মকবুল অবাক হয়ে গেল। জীবন মশায় এই কথা বলছেন? দীনুমশায়ের নাতি, জগত্মশায়ের ছেলে—জীবন মশায় এই কথা বলছেন? যে নাকি নাড়িতে হাত দিলে মকবুলের মনে হয়, অর্ধেক রোগ ভাল হয়ে গেল, তার মুখে এই কথা!
ডাক্তার তার মুখের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ হাসি হেসে, তাকে বুঝিয়েই বললেন–আমার আর ভাল লাগছে না মকবুল। তা ছাড়া বয়স হয়েছে, ভুল-ভ্ৰান্তি হয়।
–অ ডাক্তার! বলি, তুমি চিকিৎসা ছাড়লে আমাদের কী হবে হে? আমরা যাব কোথায়? নাও-নাও। লোকের হাত দেখে বিদেয় কর। তোমার ভুল-ভ্ৰান্তি! কী বলে, তোমার ভুল-ভ্রান্তি হলে সে বুঝতে হবে আমাদের অদৃষ্ট ফের! নতুন চিকিৎসা, নতুন ডাক্তার অনেক সরঞ্জাম, বৃহৎ ব্যাপার, ওসব করাতে আমাদের সাধ্যিও নাই, এতে আমাদের বিশ্বাসও নাই।–বললে কামদেবপুরের দাঁতু ঘোষাল। অনেক কষ্টেই বললে।
একসঙ্গে এতগুলি কথা বলে অনর্গল কাশতে শুরু করে দিলে সে। বুকের পাঁজরাগুলি সেই কাশির আক্ষেপে কামারের ফুটো হাপরের মত শব্দ করে উঁপছে। মনে হচ্ছে, কখন কোন মুহূর্তে দম বন্ধ হয়ে দাঁতু মাটিতে লুটিয়ে পড়বে। ডাক্তার চারিদিকে তাকিয়ে খুঁজলেন একখানা পাখা অথবা যা হোক একটা কিছু যা দিয়ে একটু বাতাস দেওয়া যায়। দতুর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে। কিন্তু কিছুই নাই কোথাও। ওই নন্দ হতভাগার জন্যে কিছু থাকবার যো নাই। শিশি-বোতল থেকে মিনিমগ্লাস, মলম তৈরির সরঞ্জাম, থারমোমিটারের খোল, এমনকি পুরনো বাতিল স্টেথোসকোপের রবারের নলের টুকরো দুটো পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছে হতভাগা। কিছু না পেয়ে ডাক্তার উঠে ভাঙা আলমারির ভিতর থেকে টেনে বের করলেন একখানা পুরনো হিসাবের খাতা; লাখ টাকা পাওনার তামাদি দলিল; তারই একদিকের খেরোর মলাটখানা ছিঁড়ে নিয়ে বাতাস দিতে শুরু করলেন। বাইরে সমাগত রোগীদের দিকে তাকিয়ে একজনকে বললেন– বাড়ি থেকে এক গ্লাস জল আন তো! চট করে।
কামদেবপুরের এই বৃদ্ধ দাঁতু ঘোষালের চিরকাল একভাবে গেল। দাঁতু যত লক্ষ্মীছাড়া তত লোভী; দুনিয়া জুড়ে খেয়ে খেয়ে লোভের তৃপ্তি খুঁজে বেড়ালে সারাজীবন; কিন্তু তাতে ললাভের তুষ্টি হয় নি, হয়েছে রোগ, পুষ্টির বদলে হয়েছে দেহের ক্ষয়। তার উপর গাঁজা খায় দাঁতু! এককালে গাঁজা খেত ক্ষুধার জন্য। গাঁজায় দম দিয়ে খেতে বসলে পাকস্থলীটি নাকি বেলুনের মত ফেপে ওঠে। তাতে আহার্য ধরে বেশি পরিমাণে। তাঁর বাড়িতেই দাঁতু ঘোষাল নিমন্ত্রণ খেতে বসে অন্ন-ব্যঞ্জনে বালতিখানেকেরও উপর কিছু উদরস্থ করে—মিষ্টির সময় সাতচল্লিশটি রসগোল্লা খেয়ে উঠেছে। জ্যৈষ্ঠ মাসে গোটা কাঁঠাল খেয়ে দাঁতু ঘোষাল যে কতবার বিছানায় শুয়ে ছটফট করেছে তার হিসেব নাই। বারচারেক তো কলেরার লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। তবু ঘোষাল লোভ সংবরণ করতে পারলে না। এখন বদহজম থেকে হাঁপানি হয়েছে। তার ওপর নেশা। গাঁজায় দম দিয়ে কো হাতে বসবে, টানবে আর কাশবে। কাশতে কাশতে হাঁপাতে শুরু করবে। এবং সপ্তাহে দুদিন ডাক্তারের এখানে আসবেওষুধ দাও ডাক্তার। ভাল ওষুধ দাও। আর ভুগতে পারছি না।
ভাল ওষুধ চায় ঘোষাল, কিন্তু মূল্য দিয়ে নয়। বিনা মূল্যে চায়। বাল্যকালে ঘোষাল জীবন ডাক্তারের সঙ্গে পাঠশালায় পড়েছিল, অনেক মন্দবুদ্ধি এবং মন্দকর্মে মতি সে যুগিয়েছে, সেই দাবিতে ডাক্তারের চিকিৎসায় ঔষধে তার অবাধ অধিকার। তার ওপরে ঘোষাল যজমানসেবী পুরোহিত ব্রাহ্মণ। অশুদ্ধ মন্ত্ৰ উচ্চারণ করে দেবতার পূজা করে বেড়ায়। সে হিসেবেও তার এ দাবি আছে। বিদেশী ডাক্তারেরা এ দাবি মানে না। তারা না মানতে পারে কিন্তু জীবন মানবে না কেন? এ দাবি তারা দীনবন্ধু মশায়ের আমল থেকে চালিয়ে আসছে, ছাড়বে কেন? তবে গুণও আছে ঘোষালের। কোনো যজ্ঞিবাড়ি থেকে কাকের মুখে বার্তা পাঠিয়ে দাও, ঘোষাল এসে হাজির হবে। কোমর বেঁধে দিবারাত্রি খেটে কাজ সেরে খেয়েদেয়ে বাড়ি যাবে। দক্ষিণা দাও ভালই, না দাও তাতেও কিছু বলবে না সে; পুরিয়া দুয়েক অর্থাৎ দু আনা কি চার আনার গাঁজা দিলেই ঘোষাল কৃতার্থ। আরও আছে, শ্মশানে যেতে ঘোষালের জুড়ি নাই। সে হিসেবে ঘোষাল এ অঞ্চলে সকলজনের একজন বান্ধব তাতে সন্দেহ নাই। উৎসবে আছে, শ্মশানে আছে–রাজদ্বারেও আছে ঘোষাল; মামলায় সে পেশাদার সাক্ষী।
সুস্থ হতে ঘোষালের বেশ কিছুক্ষণ লাগল। হেউ-হেউ শব্দে ঢেকুরের পর ঢেকুর তুলবার। চেষ্টা করে অবশেষে দু-তিনটে বেশ লম্বা এবং সশব্দ ঢেকুর তুলে একটা লম্বা নিশ্বাস নিয়ে ঘোষাল বললে—আঃ, বাঁচলাম! তারপর আবার বললে—তুমি বরং ওদের হাত দেখে শেষ কর ডাক্তার। আমি আর একটু জিরিয়ে নিই।
এই সুযোগে মকবুল এগিয়ে এল, হাত এগিয়ে দিল। ডাক্তার তার হাতখানি ধরলেন। বিচিত্ৰ হাস্যে তার মুখখানি প্রসন্ন হয়ে উঠল। উপায় নাই। তিনি ছাড়তে চাইলেও এরা তাকে ছাড়বে না; এই মকবুলেরা। নূতনকে এরা ভয় করে তাকে গ্রহণ করার মত সামর্থ্য তাদের নাই; মনেও নাই; আর্থিক সঙ্গতিতেও নাই। মকবুলের দেহ পর্যন্ত বিচিত্র। এক গ্রেন কুইনিন খেলে মকবুলের ঘাম হতে শুরু হয়, শেষ পর্যন্ত নাড়ি ছাড়ে। মকবুল বিলিতি ওষুধকে বিষের মত ভয় করে। একে একে রোগীদের দেখে তাদের ব্যবস্থা দিয়ে সবশেষে দেখলেন দাঁতু ঘোষালকে।
ঘোষাল বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে এরই মধ্যে। এবার সে হাতখানি বাড়িয়ে দিলে। জীবন ডাক্তার বললেন–তোর হাত দেখে কী করব ঘোষাল? রোগ তো তোর ভাল হবার নয়। তোর আসল রোগ হল লোভ। লোভ তো ওষুধে সারে না। তার ওপর নেশা। সকালে উঠেই এই অবস্থায় তুই গাঁজা টেনে এসেছিল।
দাঁতু লজ্জিত হয় না, সে বেশ সপ্রতিভভাবেই বললে, গাঁজাতে হয় নাই দত্ত। বিড়ি। বিড়ি। বিড়িতে হল। তোমার দাওয়াতে বসে ছিলাম, দেখলাম ওই কি বলে তাহের শেখ বিড়ি টানছে। ভারি পিপাসা হল, ওরই কাছে একটা বিড়ি নিয়ে যেই একটান টেনেছি, অমনি বুঝেছ। কিনা, হাঁপ ধরে গেল। তারপরেতে তোমাকে কতকগুলো কথা একসঙ্গে বলেছি আর ব্যস, হঠাৎ বুঝেছ কিনা–।
হাত দুটি নেড়ে দিলে দাঁতু ঘোষাল—এতেই বুঝিয়ে দিলে যে আচমকা রোগটা উঠে পড়ল। এতে আর তার অপরাধটা কোথায়? ঘোষাল নিরপরাধ ব্যক্তির মতই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—এ সব গ্রহের ফের, বুঝলে না! তা দাও ভাই, যা হোক একটা এমন ওষুধ দাও। যাতে হাঁপানি-কাশিটা কমে। সকালে বিকেলে চায়ের সঙ্গে দুটো করে চারটে আরসুলা সিদ্ধ করে করে খাচ্ছি, তাতেও কিছু হচ্ছে না।
ডাক্তার বললেন–গাঁজা-তামাক বন্ধ করতে হবে। লোকের বাড়ি খাওয়া বন্ধ করতে হবে। একেবারে ঝোল আর ভাত। না হলে ওষুধে কিছু হবে না, ওষুধও আমি দেব না ঘোষাল।
—তবে আর একবার ভাল করে হাতটা দেখ। ঘোষাল হাতটা বাড়িয়ে দিলে।দেখ, দেখে বলে দাও কবে মরব। নিদান একটি হেঁকে দাও। ওতে তো তুমি বাক-সিদ্ধ। দাও। শুনলাম কামারবুড়িকে নিদান হেঁকে দিয়েছ। গঙ্গাতীরে যেতে বলেছ। আমাকে দাও।
ডাক্তার চমকে উঠলেন। নতুন করে মনে পড়ে গেল সকালবেলার কথা। তিনি চঞ্চল হয়ে নড়েচড়ে বসে বললেন–তুই থাম ঘোষাল, তুই থাম।
তিনি তাড়াতাড়ি একখানা কাগজ টেনে প্রেসক্রিপশন লিখে ঘোষালের হাতে দিয়ে। বললেন–এই নে। গাছ-গাছড়া শুধু, দু-তিনটে জিনিস মুদিখানায় কিনে নিবি। তৈরি করে নিয়ে খাস।
ডাক্তার উঠে পড়লেন। চেয়ারখানা ঠেলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।
বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল অমরকুঁড়ির পরান খ্ৰী। সে সেলাম করে দাঁড়াল। সামনে ছইওয়ালা গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। খয়ের তৃতীয়পক্ষের স্ত্রীর দীর্ঘস্থায়ী অসুখ। আজ ছ মাস বিছানায় পড়ে আছে। মৃত সন্তান প্রসব করে বিছানায় শুয়েছে। সপ্তাহে দুদিন করে পরান ডাক্তার নিয়ে যায়। আজ যাবার দিন। যেতে হবে। পরান খ অবস্থাপন্ন চাষী। নিয়মিত ফি দিয়ে থাকে। ডাক্তার হাসলেন। একটা কথা মনে পড়ে গিয়েছে। এইসব বিনা ফি-এর রোগীদের তিনি যখন বলেছিলেন আর তাদের চিকিৎসা করবেন না তখন তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন, চিকিৎসা ছাড়লে চলবে কী করে? বাঁচতে হবে তো! আজ যে তিনি প্রায় সর্বস্বান্ত। একা তিনি নন-ঘরে স্ত্রী আছে। ক্ষমাহীনা স্ত্রী।
পরান বললে—দেরি হবে নাকি আর!
–নাঃ, দেরি কিসের। ডাক্তার পা বাড়ালেন।–চল।
পরান এদিক ওদিক তাকিয়ে বললে—আপনি তা হলে গাড়িতে চড়েন। আমি পায়দলে তুরন্ত গিয়া ধরব গাড়ি। একটু অপ্রস্তুতভাবেই বললে—কিছুটা তরি নিয়া এসেছিলাম। নন্দ নিয়া গেছে ভিতরে। ডালাটা নিয়াই যাব আমি।
পুরনো কালের লোক পরান; এখনও ভালবাসার মূল্য দেয়। ক্ষেতের ফসল, পুকুরের মাছ। ডাক্তারের বাড়ি মধ্যে মধ্যে পাঠায়। কখনও নিজেই নিয়ে আসে। বিবির অসুখে এই ভেট পাঠানোর বহরটা একটু বেড়েছে। ডাক্তারের ওপর অগাধ বিশ্বাস পরানের। নতুন কালের। চিকিৎসায় বিশ্বাস থাক বা না-থাক, নতুন কালের অল্পবয়সী ডাক্তারদের ওপর বিশ্বাস তার নাই। তৃতীয়পক্ষের বিবি যুবতী, মেয়েটি শ্রীমতীও বটে; এর ওপর পরানের আছে সন্দেহবাতিক। বিবিকে বাঁচাবার জন্য তার আকুলতার সীমা নাই, অর্থব্যয় করতেও কুণ্ঠিত নয়, কিন্তু জেনানার আবরু জলাঞ্জলি দিয়ে বাঁচার চেয়ে মরাই ভাল। জীবন মশায়ের কথা আলহিদা। পরান আলাদা শব্দটাকে বলে আলহিদা। মাথার চুল সাদা হয়েছে, চোখের চাউনির মধ্যে বাপ-চাচার চাউনি ফুটে ওঠে, গোটা মানুষটাই শীতকালের গঙ্গানদীর জলের মত পরিষ্কার।
গাড়ি মন্থর গমনে চলল।
পরান খাঁয়ের মত ঘরকয়েক বাঁধা রোগীর জন্যই মশায় সংসারের ভাবনা থেকে নিশ্চিন্ত। বর্ষায় ধানের অভাব হলে ধান ঋণ দেয় তারা। অভাব-অভিযোগের কথা জানতে পারলেই পূরণ করে। অথচ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন ডাক্তার।
কী না ছিল?
মাঠের উপর এসে পড়েছিল গাড়িটা। চারিপাশের উৎকৃষ্ট ক্ষেতগুলির দিকে আপনি চোখ পড়ল। এগুলির অধিকাংশই ছিল মশায়দের। ওই বিরাট পঁজার পুকুর, ওই শ্ৰীলাইকার, ওই ঘোষের বাগান! শুধু জমি পুকুরই নয়—এই গ্রামের সামান্য জমিদারি অংশও কিনেছিলেন তাঁর বাবা জগদ্বন্ধু মশায়। এক আনা অংশ তিনি চড়া দামে কিনেছিলেন।
গাড়ির মধ্যে বসে যেতে যেতে মনে পড়ে গেল পুরনো কথা।
তখন তাঁর কিশোর বয়স।
পড়তেন নবগ্রাম মাইনর স্কুলে। সেইবারই তার মাইনর স্কুলে শেষ বৎসর। সে আমলে জমিদারত্বের একটা উত্তাপ ছিল। যে জমিদারি কিনেছে সেকালে তারই মেজাজ পাল্টেছে। জমিদারি কিনলেই লোকে মনে করত-লক্ষ্মী বাধা পড়লেন। সে আমলের প্রসিদ্ধ যাত্ৰাদলের অধিকারী কণ্ঠমহাশয়ের গানে আছে—আগে করবে জমিদারি তবে করবে পাকাবাড়ি। তারই স্বজাতি জ্ঞাতি ঘোষগ্রামের রাধাকৃষ্ণ মিত্র ওই নবগ্রাম মাইনর স্কুলে পড়ত। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা নবগ্রামের প্রতিপত্তিশালী জমিদারের ভাইয়ের সঙ্গে চলত তার অবিশ্রাম প্রতিযোগিতা। লেখাপড়ায় নয়, জমিদার-বংশধরত্বের। প্রায়ই খিটিমিটি বাঁধত। বাবার মূলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাকত রাধাকৃষ্ণ। বলত, He is a Zaminders son, I am also a Zaminders son; এখন ঝগড়া হচ্ছে, বড় হলে দাঙ্গা হবে।
তাঁর বাবা জগদ্বন্ধু জমিদারি কেনার পর তার মনে এ উত্তাপ কিছুটা সঞ্চারিত হয়েছিল। লোকে সহপাঠীরা—বলেছিল, গুলবাঘা এবার ডোরাবাঘা হল! সাবধান!
সহপাঠীরা তাঁকে বলত–গুলবাঘা।
সেই কিশোর বয়সে তাঁর নিজের রূপের কথা মনে পড়ছিল। রূপ—যে রূপ সুকুমারকোমল-উজ্জ্বল—সে রূপ তার কোনোকালে ছিল না। কিন্তু রূপ তাঁর ছিল। সবল পরিপুষ্ট দেহ-গোল মুখ, ঝকঝকে চোখ, নির্ভীক দৃষ্টি, শ্যামবর্ণ দুর্দান্ত কিশোর। হাড়ু-ড়ু-ড়ু খেলবার সময় মালকোচা মেরে জীবন ডাক দিতে ছুটলে প্রতিপক্ষ দল খানিক পিছিয়ে থোল অর্থাৎ স্থল নিত। বলত-হাঁ গুলবাঘা ছুটেছে।
এধার থেকে ওধার মুহূর্তে ছুটে ঘুরবার ভান করে একেবারে মাঝের দাগের কাছে পর্যন্ত এসে বোঁ করে আবার ঘুরে আক্রমণ করতেন। কাউকে না কাউকে মেরে আবার ঘুরতেন।
বাড়ির পিছনে কুস্তির আখড়া ছিল। ল্যাঙট পরে নরম মাটির উপর দেহ ঠুকে আছাড় খেতেন শরীর শক্ত করবার জন্য। এর ওপর মুগুর ছিল, সে দুটো আজও আছে।
গুলবাঘ হিংস্রতর নরঘাতী ডোরাবাঘই হয়ে উঠত যদি না জগদ্বন্ধু মশায় মাথার উপরে থাকতেন। জগদ্বন্ধু মশায়ের চিত্ত এতে বিন্দুমাত্র উত্তপ্ত হয় নি। মশার বংশের মহাশয়ত্বই ছিল তার কাছে সবচেয়ে বড়। দম্ভের মোহে তিনি জমিদারি কেনেন নি। জমিদারির ওপর কোনো মোহ তার ছিল না। জমিদারি তিনি কিনেছিলেন জমিদারের দম্ভের উত্তাপ থেকে বাঁচবার জন্য। যেদিন জমিদারি কেনা হয় সেদিনের একটা কথা মনে পড়ছে।
জগদ্বন্ধু মশায়ের বন্ধু, পেশায় গোমস্তা ঠাকুরদাস মিশ্ৰ যে চিকিৎসালয়ের দেওয়ালে লিখেছিল লাভানাং শ্ৰেয় আরোগ্যম্, সে-ই তাঁকে শ্লেষ করে বলেছিল—তা হলে এবার জমিদার হলে। আশয়ের চেয়ে বিষয় বড় হল। আগে লোকে সম্ভ্রম করত—মশায় বলে, এবার লোক প্রণাম করবে জমিদার মশায় বলে! বাবুমশায় বলে! ঠাকুরদাস বাতের যন্ত্রণা এবং আরোগ্যের আনন্দ তখন একেবারেই ভুলে গেছে। অনেক দিন হয়ে গেছে তখন।
জগদ্বন্ধু বলেছিলেন—ভাই, ঢাল আর তরোয়াল দুটোই হল অস্ত্র। ওর একটা থাকলেই সে যোদ্ধা। কিন্তু তরোয়াল না নিয়ে তরোয়ালের চোট থেকে মাথা বাঁচাতে শুধু ঢালটা যে রাখে তাতে আর তরোয়ালধারীতে তফাত আছে। আছে কি না আছে—তুমিই বল। ঠাকুরদাস, ওটা আমার ঢাল, শুধু ঢাল। নবগ্রামের তরোয়ালধারী জমিদারদের উঁচানো তরেয়ালের কোপ থেকে আশয়ের মাথা বাঁচানো দায় হয়ে উঠেছিল। তাই ঢাল অস্ত্র হলেও ধরতে ল। কথাটা তোকে খুলেই বলি ঠাকুরদাস। নবগ্রামের জমিদারদের কাছে মান বজায় রাখা দায় হয়ে উঠেছে ভাই। সদাই ওঁরা শস্ত্ৰপাণি। নবগ্রামের রায়চৌধুরী বংশের তরোয়াল ভঙেছে, ওঁরা এখন বাট ঘুরিয়ে তারই ঘায়ে লোকের মাথা ভাঙতে চান। আবার নতুন ধনী ব্ৰজ লালবাবু এখন আমাদের গ্রামের আট আনা অংশের জমিদার। তাদের হল চকচকে ধারালো তরোয়াল। আজ মাসছয়েক থেকে দেখছি, ব্ৰজবাবুদের বাড়িতে অসুখবিসুখ হলে ডাক আসছে চাপরাসী মারফত। সেলাম অবিশ্যি করে। বলে—সালাম গো ডাক্তারবাবু বাবুদের বাড়ি একবার যেতে হবে যে। ওদের দেখাদেখি রায়চৌধুরীরা পথে-ঘাটে দেখা হলে হেঁকে বলতে শুরু করেছে—মশায় হে, একবার আমাদের বাড়ি হয়ে যাবে যেন। তবু তো বড়বাবুরা দর্শনী দেন, এরা আবার তাও দেয় না। বুঝেছ না, অনেক ভেবে ঢাল কিনলাম। এ আমার তরোয়াল নয়। এক হাতে ঢাল থাকল অন্য হাতে খলনুড়ি। ওটা ছাতার বদল।
কথাটা তিনি তার জীবনে সত্য বলেই প্রমাণিত করেছিলেন। তার ওই ঢালের আড়ালে এ গ্রামের অনেক জনকে তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। এবং ওই ঢাল দেখিয়ে এ গ্রামের কাউকে কখনও অস্ত্রধারীর ঔদ্ধত্য অপমানিত করেন নি।
কথাগুলি জীবন দত্ত নিজের কানে শুনেছিলেন। পাশের ঘরেই তিনি বসে পড়ছিলেন সেদিন।
তবুও জীবন মশায়ের মনে বিষয়-বৈভবের দম্ভের উত্তাপ সঞ্চারিত হয়েছিল। কী করবেন তিনি? উত্তাপ লাগলে উত্তপ্ত হওয়া যে প্রকৃতি-ধর্ম। এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া তো সহজ নয়। নইলে তিনি ডাক্তার হতেন না। বাপের কাছে কবিরাজিই শিখতেন। উত্তপ্ত বস্তু সহজ ধর্মে আয়তনে বাড়তে চায়। জমিদারের এবং বড়লোকের ছেলে তার বৈভব ও অহঙ্কারের উত্তপ্তচিত্ত তখন বাপপিতামহের জীবনপরিধিকে ছাড়িয়ে বাড়তে, বড় হতে চাচ্ছে! তাই জগদ্বন্ধু ছেলের মাইনর পড়া শেষ হওয়ার পর তাকে টোলে ভর্তি করতে চাইলেন। ব্যাকরণ শেষ করার পর আয়ুৰ্বেদ পড়বে। কিন্তু জীবন মশায় বলেছিলেন আমার ইচ্ছে ডাক্তারি পড়ি।
—ডাক্তারি!
–হ্যাঁ। দেশে তো ডাক্তারিরই চলন হতে চলল। কবিরাজিতে লোকের বিশ্বাস কমে যাচ্ছে। বর্ধমানে স্কুল হয়েছে। আমি ওখানেই পড়ব।
দেশে সত্যই তখন ডাক্তারি অর্থাৎ অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা রাজকীয় সমারোহে রথে চড়ে আবির্ভূত হয়েছে। কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ, হাসপাতাল, বর্ধমান মেডিক্যাল স্কুল, জেলার সদরে সদরে হাসপাতাল, চ্যারিটেবল ডিসপেনসারি, ইংরেজ সাহেব ডাক্তার, দেশী নামজাদা ডাক্তারদের পোশাক গলাবন্ধ কোট, প্যান্টালুন, গোল টুপি, গার্ডচেন, বার্নিশ-করা কাঠের কলবাক্স; ঝকঝকে লেবেল ঝাঁটা সুন্দর শিশিতে ঝাজালো রঙিন ওষুধ, ওষুধ তৈরির সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া, সব মিলিয়ে সে যেন একটা অভিযান। এ অঞ্চলে তখনও কবিরাজির রাজ্য চলছে। এ যুগের সঁড়াশি আক্রমণের মত দুদিকে বসেছেন দুজন ডাক্তার। উত্তর এবং দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। উত্তরে বসেছেন ভুবন ডাক্তার। বড় লাল ঘোড়ায় চেপে ব্রিচেস আর গলাবন্ধ কোট পরে ভুবন ডাক্তার মধ্যে মধ্যে এ পথে যাওয়া-আসা করেন। আর উত্তর থেকে আসেন রঙলাল ডাক্তার তসরের প্যান্টালুন, গলাবন্ধ কোট, গলায় ঝোলানো পকেটঘড়ি। রঙলাল ডাক্তার যাওয়া-আসা করেন পালকিতে। রঙলাল ডাক্তার থাকেন এখান থেকে মাইল চারেক দূরে। এ অঞ্চলে তিনিই প্রথম অ্যালাপ্যাথি নিয়ে এসেছেন। অদ্ভুত চিকিৎসক। প্রতিভাধর ব্যক্তি। মেডিক্যাল কলেজ বা স্কুলে তিনি পড়েন নি; নিজে বাড়িতে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। নদী থেকে, শ্মশান থেকে শব নিয়ে এসে গ্রন্থের নির্দেশ অনুসারে কেটে অ্যানাটমি শিখেছেন। বিস্ময়কর সাধনা। তেমনি সিদ্ধি। কোথায় বাড়ি হুগলী জেলায়, সেখান থেকে এসেছিলেন এ জেলায় রাজ হাই ইংলিশ স্কুলে শিক্ষকতার কর্ম নিয়ে। ইংরিজিতে অধিকার ছিল নাকি অসামান্য। আর তেমনি ছিল অগাধ আত্মবিশ্বাস। বিখ্যাত হেডমাস্টার শিববাবুর ইংরিজি খসড়া দেখে দু-এক জায়গায় দাগ দিয়ে বলতেন—এখানটা পালটে এই করে দিন। ইমপ্রুভ করবে! বলতে সঙ্কোচ অনুভব করতেন না। তিনি হঠাৎ কোনো আকর্ষণে ময়ূরাক্ষী-তীরে নির্জন একটি গ্রামে এসে এই সাধনা করেছিলেন। তপস্বীর মত। তারপর একদিন বললেন–এইবার চিকিৎসা করব। এবং কিছুদিনের মধ্যেই এ অঞ্চলে অসামান্য প্রতিষ্ঠালাভ করলেন। রঙলাল ডাক্তারের চিকিৎসার খ্যাতি রঙলালকেই প্রতিষ্ঠা দেয় নি—তাঁর সঙ্গে অ্যালোপ্যাথিরও প্রতিষ্ঠা করেছিল। চারিদিকে নতুন চিকিৎসার প্রতি মানুষ শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে শুরু করলে।
জীবন ডাক্তার সেদিন কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে কবিরাজির পরিবর্তে ডাক্তারির প্রতি আকৃষ্ট হলেন। প্রতিষ্ঠা চাই, খ্যাতি চাই, অর্থ চাই, মানুষের কাছ থেকে অগাধ শ্রদ্ধা চাই। তার প্রেরণা দিয়েছিল ওই জমিদারিটুকু। জমিদারি যখন কিনেছেন বাবা তখন অবশ্যই পারবেন ডাক্তারি পড়াতে। তাই মাইনর পাস করে তিনি গেলেন কাঁদী রাজ হাই স্কুলে এন্ট্রান্স পড়তে। এন্ট্রান্স পাস করে এফ. এ. পড়বেন, তারপর ডাক্তারি।
* * * * *
গরুরগাড়িটা থামতেই ডাক্তারের তন্ময়তা ভেঙে গেল। সামনেই পরান খাঁয়ের দলিজা। এসে পড়েছেন। পুরনো কাল থেকে বাস্তব বর্তমানও বটে।