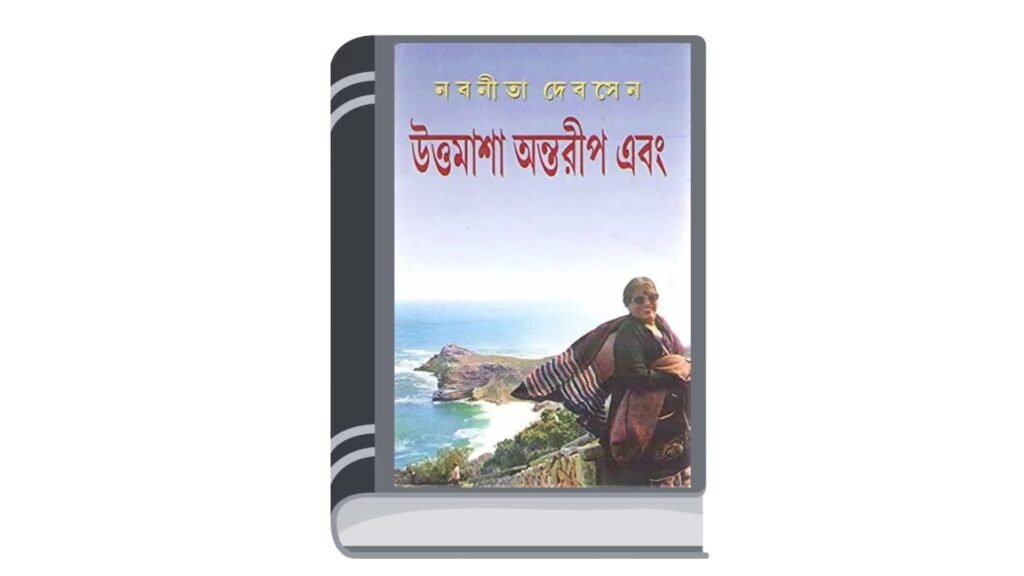প্রথম পর্ব – ২০০৭
ডারবান ডায়ারি
বিনা ভনিতায় বললে, আমার মনে হয় ডারবানে না এলে, একজন ভারতীয়ের পক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকাতে আসার কোনও মানে হয় না। যেদিন হঠাৎ ঠিক হল নন্দনার নেমন্তন্নে ওর সঙ্গে দশদিনের মধ্যেই আমি দক্ষিণ আফ্রিকাতে বেড়াতে যাব, কিন্তু তার ছবির শুটিং শুধুই কেপটাউনে, সেদিন থেকে চেষ্টা করেছি কী উপায়ে ডারবানে যাওয়া যায়। কাউকেই চিনি না সেখানে। আমাদের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর স্বামী ওখানে একদা রাষ্ট্রদূত ছিলেন, বাঙ্গালোরে ফোন করে বন্ধুকেই জিজ্ঞেস করি কাউকে চেনে কিনা।
বন্ধু তো শুনেই আহ্লাদে আটখানা হয়ে ফোনে যত লাফানো যায় ততটা লাফিয়ে উঠে বললে সে নিজেই যাচ্ছে ঠিক ওই সময়েই, ডারবানে একটা আন্তর্জাতিক নারী-সমাবেশে ওর বক্তৃতা আছে। আমি যেন বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে ডারবানের টিকিট কিনে ফেলি, ওর ঘরেই থাকতে পারব, ওর সঙ্গে কনফারেন্সেও যেতে পারব, সেখানে উইনি ম্যাণ্ডেলা একজন বক্তা, আরো কত আফ্রিকার নারীবাদী নেত্রীদের সঙ্গে দেখা হবে। আফ্রিকার নৃত্য-গীত হবে, অসাধারণ অভিজ্ঞতার সুযোগ। কিন্তু ব্যস্ততার মধ্যে আমাকে ডারবান ঘোরানোর সময় পাবে না সে।
আমি বলি তাতে কি, আমি টুরিস্টের বাসে ঘুরে নেব, গান্ধিজির স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলি ছাড়া আর কিছু তো আমার দ্রষ্টব্য নেই।
মেয়েরাও উত্তেজিত, নন্দনা হৈ হৈ করে কেপটাউনের টিকিট বদলে জোহানেসবর্গ থেকে ডারবানের টিকিট করে ফেলল। যদিও আলাদা করে গচ্চা দিয়ে ডারবান থেকে কেপটাউনের নতুন টিকিট কিনতে হল, আগের টিকিটে দুবার পথিমধ্যে থামা যাবে না। টুম্পুশি সোজা জোহানেসবর্গ থেকে চলে যাবে কেপটাউনে। আমি ডারবান। আমার জন্য বন্ধুটি ডারবানের এয়ারপোর্টে গাড়ি পাঠাবে। ও আগের দিন পৌঁছোবে, আমি আর টুম্পুশি যেদিন জোবর্গে নামছি (জোহানেসবর্গের আদুরে ডাকনাম) সেদিনই সে নামছে ডারবানে। একই দিনে আমারা রওনা হচ্ছি, আমরা মম্বুই থেকে, সে বেঙ্গালুর থেকে। ১৮ই রাত্রে এই ব্যবস্থা পাকা হল।
আমার আনন্দ রাখবার জায়গা নেই, আর বান্ধবীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় সমস্ত হৃদয় নুয়ে পড়ল। চেয়েছিলুম শুধু কয়েকটা ঠিকানার খোঁজ, একেবারে সব ব্যবস্থা করে দিল। এই নাহলে পুরনো বন্ধু।
মুম্বই পৌঁছেছি ১৮ই গভীর রাত্রে। আমার বান্ধবীর কছে থেকে পরের দিন ১৯শে সকালে এস এম এস মেসেজ এল আমার কন্যার কাছে। টুম্পা তোমার মায়ের টিকিট ক্যানসেল করো, আমি নিজেই যাব কিনা ঠিক নেই, ওদের মিটিং হয়ে গিয়েছে, উইনির বক্তৃতা শেষ, প্রিপোন করেছে কনফারেন্স, মাকে তুমিই সঙ্গে করে কেপটাউনে নিয়ে যাও। শেষ অবধি যদিও বা আমি পরের মিটিংটাতে যাই, ডারবানে তোমার মার সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যকারী কে থাকবে? আমি গেলেও তো ব্যস্ত থাকব। এজন্যে আমি খুবই দুঃখিত, কিন্তু না, তুমি টিকিট বদল করে নাও
১৯শে সকালে এই খবর এল, ১৯শেই রাতে আমাদের যাত্রা। এখন পুনরায় টিকিট বদলের জন্য আবার অনেকগুলো টাকার ধাক্কা। সময়ই বা কোথায়? আমি বললুম আজ্ঞে না, কেউ যাক বা না যাক আমি ডারবানে যাব। এয়ারপোর্টে নিশ্চয়ই হোটেলের খবর থাকবে, একবেলার জন্যেও যাব। ওখানে টুরিস্ট বাসের ব্যবস্থা থাকবে নিশ্চয়ই। আমার ফেরার টিকিট বরং এগিয়ে দে। তিন দিন নয়, একা একা এক দিন করে দে। ক্যান্সেলেশন চার্জও লাগবে না। একটা দিন ঠিক ম্যানেজ করে নেব, এ তো অরণ্য আফ্রিকা নয়, নগর আফ্রিকা। ওইদিন রাত্রেই রওনা টিকিট হলে সব চেয়ে ভাল। ওতে হোটেলের ভাবনা নেই। মালপত্তর বিমানবন্দরে রেখে তোরা দেখিস ঠিক ঘুরে নেব।
কিন্তু মেয়ে বেঁকে বসল। অচেনা অজানা দেশে, কিঞ্চিত স্খলিত চরণে, লাঠি হাতে, মালপত্তরসমেত, অনিশ্চয়তার মধ্যে মাকে ছেড়ে দিতে মোটেই রাজি হল না টুম্পা, পরামর্শ করতে দিল্লিতে দিদিকে ফোন করল।—”দিদি, এ যদি ইউরোপ আমেরিকা হত তবে ঠিক আছে, মা ঠিক ম্যানেজ করে নিতেন, কিন্তু আফ্রিকাতে তো যান নি কোনওদিন? বিমানবন্দরে ওইভাবে চট-জলদি ব্যবস্থা ওখানে করা যায় কিনা কে জানে? আর জোহানেসবর্গের ক্রাইমরেট দক্ষিণ আফ্রিকাতে সর্বোচ্চ। ডারবানেও কি কম? মা যে গিয়েই ক্রিমিনালের পাল্লায় পড়বেন, তাতে ওর সন্দেহ নেই। ওদিকে একজনও চেনা লোক নেই এতবড় শহর ডারবানে। এখন খোঁজ-খবরের সময়ও নেই হাতে।”
কী করা যায়? মা এদিকে জেদ ধরে বসেছেন, ডারবানে যাবেনই!—দিদি তো শুনে খাপ্পা ‘সে কি? অমুকমাসি তো নিজেই যেতে বলে কালই টিকিট বদল করিয়েছেন, আর আজ সকালে ক্যানসেল করাচ্ছেন? মায়ের প্রিয় বান্ধবীর হল কী? সদ্য পদ্মভূষণ পেয়েছেন, এর মধ্যেই ভীমরতি? ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সের আবার প্রিপোনিং হয় নাকি? যে দেশে এমন অঘটনও ঘটতে পারে, সেই দেশে মা একা একা ঘুরতে যাবেন? দাঁড়া দেখি কী করা যায়। মা যখন এত যেতে চান যাওয়াই উচিত। আমার এক বন্ধু আছে বিদেশ মন্ত্রকে, দেখি সে যদি কিছু পারে।’
মেয়ে তো লেগে পড়ল মায়ের শখ মেটাতে, কিন্তু সময় কৈ? এদেশে বেলা বারোটার আগে দক্ষিণ আফ্রিকার কোনও অফিসে ফোন করা যায় না, তখন ওখানে সকাল সাড়ে আটটা বাজে। এর মধ্যে ব্যবস্থার সময় খুবই কম। আজ রাতেই আমাদের যাত্রা। হাল ছেড়ে দিয়েও ছাড়ি না। ভাবলুম, আজ ফের টিকিট বদল করে, ফের গচ্চা দিয়ে, তার পরে দেখি কেপটাউন থেকেই যদি নতুন করে ডারবানে আসার চেষ্টা করতে পারি। ওখানে তো দু-হপ্তার বেশি সময় পাচ্ছি।
লেকিন খোদা যব দেতা ছপ্পড় ফোড়কে দেতা। পিকোর বন্ধুটি অসাধ্য সাধন করে ফেললেন। সাড়ে তিনটের মধ্যে জানিয়ে দিলেন, আমার সব ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। গান্ধিজির স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলি দেখতে ভারতের একজন উৎসাহী লেখিকা আসতে চান শুনে মাননীয় কনসাল জেনারেল নিজেই আমাকে ব্যক্তিগত নিমন্ত্রণ করেছেন। তিনি দার্জিলিং-এর মানুষ, বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত। এয়ারপোর্টে তাঁর গাড়ি আসবে, তাঁরই বাড়িতে থাকব, তাঁরই গাড়িতে ফিনিক্স সেটেলমেন্ট, পিটারমারিৎসবর্গ স্টেশন, সব ঘুরিয়ে দেখাবেন তাঁর পরবর্তী উচ্চপদস্থ অফিসার, যিনি বঙ্গসন্তান, শ্রীঅরিন্দম মুখার্জি। আমার সঙ্গে আলাপের জন্য ওই সন্ধ্যায় বাঙালিদের ডেকে একটি ডিনারও দেবেন স্থির করেছেন তিনি নিজের বাড়িতে, যেহেতু কনসাল জেনারেল এদিন সন্ধ্যয় ব্যস্ত আছেন অন্যত্র। ব্যস, নিশ্চিন্ত। আর কি চাই? মেয়েদের তো আহ্লাদের অন্ত নেই, মাসির কেলোর কীর্তিতে মায়ের যাত্রা পণ্ড হয়নি, বরং বেশি ভালভাবে গুছোনো হল। দুই মেয়ের যুগ্ম প্রচেষ্টায় এবং অমিত দাশগুপ্ত আর অরিন্দম মুখোপাধ্যায়, দিল্লি এবং ডারবানে বিদেশ মন্ত্রকের এই দুই সুহৃদয় বঙ্গসন্তানের বন্ধু প্রীতি এবং সাহিত্যপ্রীতির সম্মিলিত ফলেই আমার ডারবানে যাওয়া এমন নাটকীয় ভাবে সম্ভব হল। নেহাত অপরিচিত কেপটাউনের টিকিটটা এগিয়ে ২৪শের বদলে ২২ শে করে নিলুম। একটি দিনের বেশি অচেনা অতিথির অত্যাচার সইতে না হয় যাতে মহানহৃদয় কনসাল জেনারেলকে। তা ছাড়া ২২শে কেপটাউনের কনসাল জেনারেলের বাড়িতে নৈশভোজের আমন্ত্রণ আছে নন্দনার আর আমার, নন্দনা জানিয়েছিল। আমি ভেবেছিলুম যাব না। এবার ঠিক করলুম যাব।
আর এস এম নয়, বান্ধবীর উচ্ছ্বসিত ফোন এল, ঠিক বিকেলে ৪টের সময়ে। আনন্দে উচ্ছল হয়ে সে বললে বাঃ কনগ্র্যাচুলেশন্স! আমি এখনি ডারবানের কনসুলেট থেকে খবর পেলুম কলকাতা থেকে এক লেখিকা আসছেন ওখানে, গান্ধিজির স্মারক সৌধগুলি দেখতে চেয়ে। তবে তো তোমার ব্যবস্থা হয়েই গিয়েছে, খুব মজা, গেলে দেখা হবে।
“কিন্তু দেখা কি করে হবে? তুমি নিজেই তো যাচ্ছ না।”
ইতস্তত করে বান্ধবী বললে— “শেষ অবধি আমিও যাচ্ছি, তবে আজ নয়, ১৯শে, দেরি করে, ২৩শে যাচ্ছি, ২৪শে আমার বক্তৃতা আছে। তুমি নিশ্চয়ই আমার বক্তৃতায় এস। আমি যাবার সব বন্দোবস্ত করে দেবো।”
—”কিন্তু আমি তো অতদিন থাকতে পারব না ভাই? ২১শে মাত্র একদিনের জন্যে ডারবানে যাচ্ছি। ২২শে সকালে কেপটাউনে চলে যাব। রাত্তিরে কন্সুলেটে ডিনার আছে টুম্পার সঙ্গে। তুমি ভাল করে বক্তৃতা দিয়ো। অল দ্য বেস্ট! দেশেই দেখা হবে।”
জোহানেসবর্গে ২০শে এপ্রিল
সাউথ আফ্রিকান এয়ারলাইনে এই প্রথম। অসামান্য বিজনেস ক্লাস। পুরো প্রথম শ্রেণীর সুবিধা। সোজা লম্বা হয়ে কাঠের মতো শুয়ে পড়া। ব্রিটিশ ব্রিজনেস ক্লাসেও এখন এমনি শয্যার ব্যবস্থা আছে কিন্তু এত চওড়া, এত আরামপ্রদ নয়। একটু একটু খাঁচার মতো লাগে, পর্দানশীন যেন, প্রিভেসির কারণে। এখানে খোলামেলা। আমরা ভাগ্যগুণে প্রথম সীট দুটি পেয়ে মহা আরামে এলুম। ফেরার পথেও এই সীট বুক করতে হবে।
প্রথমে জোহানেসবর্গে। দক্ষিণ আফ্রিকার সব উড়ানই এখানে প্রথম পৌঁছোয়। তার পর যেদিকে যাবে যাও। আমাদের জোহানেসবর্গে একদিনের প্রোগ্রাম একেবারে ঠাসা। প্রথমেই নন্দনার বন্ধু জেড ম্যাকেল নামে একটি ব্রিটিশ ছেলের সঙ্গে লাঞ্চ। তারপরে দৌড় দৌড় সোয়েটো। এইখানেই ৭৬এর কালো ছেলেমেয়েদের সেই রক্তক্ষরা আন্দোলন শুরু। দরিদ্র শ্রমিক কালো মানুষদের ক্রমশ ধনবান সাদারা এক সময়ে শহরের কেন্দ্র থেকে দূরে সরিয়ে দিতে শুরু করল। ট্রাকে ভরে ভরে মানুষগুলোকে মালপত্রসমেত মাঠের মধ্যে নামিয়ে দিচ্ছিল, এবারে তাদের কপালে শহরের পাকাবাড়ি ছেড়ে এসে তেপান্তরের মাঠের মধ্যে চট, টিন, কাঠ দিয়ে বস্তি বানিয়ে থাকা। বিদ্যুৎ নেই, জল নিয়ে আসতে হয় দূর থেকে। কালো শ্রমিকদের ঝোপড়পট্টি বস্তি এইভাবে আস্তে আস্তে সব শহরের প্রান্তেই গড়ে উঠেছিল, তাদের ভাল নাম টাউনশিপ। পরে অত ফ্যাশনেবল কেপটাউনেও দেখলুম নগরের প্রান্তে আমাদের অতি পরিচিত দৈন্যের দৃশ্য। আসার আগে আমাকে শ্রী গোপালকৃষ্ণ গান্ধি বলে দিয়েছেন জোহানেসবর্গে গেলে নিশচয়ই সোয়েটো যাবেন। আর পারলে নাদিন গর্ডিমারের সঙ্গে দেখা করবেন।
অতএব সোয়েটো থেকে ফিরেই সোজা উইট্স ইউনিভার্সিটিতে ছুট। দুই নোবেল লরিয়েটের মধ্যে কথোপকথনের এক উজ্জ্বল সন্ধ্যা আয়োজিত হয়েছে সেখানে, লেখিকা নাদিন গর্ডিমার, আর অধ্যাপক অমর্ত্য সেন-এর সঙ্গে থাকবেন এদেশের অর্থমন্ত্রী ট্রেভর ম্যানুয়েল এবং জাস্টিস এডউইন ক্যামেরন। তিনি উইটস্ ইউনিভার্সিটির কোর্টের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে চলেছেন দশ বছর ধরে। এবারে পুনরায় নির্বাচিত হলেন দুই বছরের জন্য। ছাত্রেরা বদল চেয়েছিল, কিন্তু ইউনিভার্সিটিতে তাঁকেই সবচেয়ে যোগ্য, ন্যায়পরায়ণ, সৎপরিচালক বলে মনে করা হয়। আজকের আলোচনার সঞ্চালক তিনিই। বিষয় দারিদ্র্য ও হিংসার যোগ এবং দারিদ্র্য-মোচনের চেষ্টার রকমসকম। জোহানেসবর্গে শুধু নয়, সারা দক্ষিণ আফ্রিকাতে বহু বিজ্ঞাপিত হয়েছে এই আলাপনী সন্ধ্যা। এর আগের দিনেই অমর্ত্য সেন এ বছরের প্রসিদ্ধ নাদিন গর্ডিমার বক্তৃতাটি দিয়েছেন দারিদ্র্য, যুদ্ধ ও হিংসা—এই বিষয়ে। সেদিন নাকি দরজায় আগ্রহী শ্রোতাদের ভীড়ে মারামারির অবস্থা হয়েছিল। আজ তাই খুব পুলিশী সতর্কতার বন্দোবস্ত থাকবে। আলোচনার পরে শ্রীমতী নাদিন গর্ডিমারের সঙ্গে এবং অন্যান্য মাননীয় আলোচকদের সঙ্গে আমাদেরও মা-মেয়ের নিমন্ত্রণ আছে একটি বিশেষ আফ্রিকান ডিনারে। পরের দিনেই আবার আমাদের বেরিয়ে পড়া। কুড়ি তারিখে পদক্ষেপ মাত্রেই আমার দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে নিগূঢ় আলাপ। আর কি প্রচণ্ড এই নক্ষত্রের যোগাযোগ। এই সময়েই মেয়ের শুটিং আর বাবার বক্তৃতা পড়েছে একই মহাদেশে। মাঝ থেকে বিনা চেষ্টাতে মায়ের কিঞ্চিত মজা।
সারাদিন সোয়েটো ঘুরে এসে আলোচনা সভাতে ঢুকতে ঢুকতেই মনে হয়েছিল মগজ দিয়ে আকাডেমিক্যালি জানলেও, হৃদয় দিয়ে জীবনে কত কী বোঝা বাকি ছিল। মাত্র একটি দিন সারাদিনে যে কত কিছু শিখতে পারে মানুষ!
এলসা • মি কাসা সু কাসা • জেড
জো বর্গের বিমানবন্দরে নামতে, এক সুন্দরী অভিজাতদর্শন মহিলা আমাদের দেখে সহাস্যে এগিয়ে এলেন, প্রফেসর দেব সেন লেখা কাগজ হাতে। তিনি আমাদের সারথি, গাড়ি এনেছেন অতিথিশালাতে নিয়ে যেতে। আমি তো ভেবেছি তিনিও অধ্যাপক। না, এটাই এলসার ব্যবসা। আমাদের অতিথিশালাটি জো বর্গের খুব ফ্যাশনেবল পল্লীতে, মেলভিলে। যত অভিজাত রেস্তোরাঁ যত ভাল জ্যাজ, যত ঝলমলে নাইটলাইফ, ধনীদের বিলাস-ব্যসনের আর অল্পবয়সীদের ঘুরে বেড়াবার জায়গা এই মেলভিল। সপ্তাহান্তে রাত্রি নামে না এখানে, শুক্র-শনিবার সারা রাত জাগে মেলভিল। আমার জ্যাজে চিরকালের আকর্ষণ। অন্তরা নন্দনারও তাই জ্যাজে স্বাভাবিক রুচি হয়েছে। শ্রাবস্তীর অবশ্য আর্বান ফোকে যত আগ্ৰহ জ্যাজে ততটা উৎসাহ নেই। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও এবং আজ যদিও শুক্রবার, আমাদের আজকের রুটিনে, হায়, মা-মেয়ের নিশাচরীপনার সুযোগ নেই। ভোরে বেরুতে হবে।
যে সুন্দর অতিথিশালাটিতে এলুম, দেখেই মন ভরে গেল। যেন ইতালি বা স্পেনের কোনও গ্রামের বাড়িতে এসেছি। নামওতাই, আমার বাড়ি তোমার বাড়ি। মি কাসা সু কাসা ভিতরে ঢুকলে ছোট্ট এবড়োখেবড়ো পাথরের উঠোনের মধ্যিখানে তেমনই রুক্ষ পাথরের ফোয়ারার ঠাণ্ডা জল ঝরছে। পাথুরে পাঁচিলের দেওয়ালে ফুলভরা লতাপাতা উঠেছে। দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। আরো একটু ভিতরে গেলেই পাঁচতারার মতো আরাম। সুইমিং পুলেরও অভাব নেই। ঘরে ঢুকেই ভাল লাগে, এত খোলামেলা, গুচ্ছ গুচ্ছ তাজা ফুল দিয়ে সাজানো। ধবধবে বিছানার ওপরে দুটি সুগন্ধী ল্যাভেণ্ডার ফুলের মঞ্জরী আড়াআড়ি করে রাখা, তাদের কেন্দ্রে একটি চকোলেট। আমার আর টুম্পুশির দুটি ঘরের মাঝখানে একটি নিজস্ব চমৎকার বারান্দা, সামনে সুইমিং পুল তার ওপারে ছোট ছোট টিলার ঢেউ। ভিতরে চারদিকে সবুজ, অনেক রকমের পাতার বাহার।
স্নান সেরে নিয়ে তৈরি হতেই জেড আর তার স্ত্রী কন্যা এসে গেল, নন্দনার বন্ধু সুজানের ভাই। বাড়ির কাছে খুব চমৎকার একটি স্প্যানিশ রেস্তোরাঁতে খেতে গেলুম। জেড়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে দক্ষিণ আফ্রিকার অতীত ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে একটি যারপরনাই উপকারী স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি পেলুম। সাদা হলেও এই উদার বামপন্থী ইংরেজ যুবকের চোখে দক্ষিণ আফ্রিকার ছবি যেভাবে বিম্বিত সেটি আমার যথেষ্ট নিরপেক্ষ, সুচিন্তিত, যথার্থ এবং গ্রহণযোগ্য মনে হল। জেড আগে ভারতীয় কোম্পানি ইউনিলিভার-এর কর্মী ছিল দক্ষিণ আফ্রিকাতে। অনবদ্য স্প্যানিশ রান্না খেতে না খেতেই সোয়েটো যাত্রার সময় হয়ে গেল। জেডের সঙ্গে আরো কথা বললে ভাল লাগত। কিন্তু আমাদের এই দুর্দিনের যাত্রাগুলি এরকমই অসম্পূর্ণ সম্পর্কের ছিন্ন মালিকা।
সোয়েটো সোফিয়া
সোয়েটো যাওয়ার গাড়ি নিয়ে অতিথিশালার সামনে দাঁড়িয়েছিল সোফিসো। শ্রাবস্তীর বন্ধু অরিজিতের বন্ধু জিজ্ঞাসা, সে এই ব্যবস্থা করে রেখেছে। শুনতে আফ্রিকান শব্দের মতো শোনালেও আসলে সোয়েটো নামটি ইংরেজি থেকে। তিনটি শব্দ থেকে দুটি করে অক্ষর নিয়ে তৈরি। SOWETO=South Western Township.
সেখানে সোনার খনির শ্রমিকদের বস্তি। পথ তেমন সুন্দর কিছু নয়। কিন্তু সারথি সুন্দর। কালো ঝকঝকে সপ্রতিভ তরুণ সোফিসোর সঙ্গে কথা কইতে ভাল লাগে।
–তোমার নামের মানে আছে? সোফিসা?
–বা থাকবে না? সব আফ্রিকান নামের মানে থাকে। সোফিসা মানে হচ্ছে, উইশ। সোফিসো সগর্বে বলে তিন বোনের পরে আমি ছেলে জন্মেছিলুম কিনা, বাবা মায়ের ইচ্ছাপূরণ করে তাই আমার নাম সোফিসা।
–বাঃ বেশ তো? তোমার তৃতীয় দিদির নাম কী, সোফিসা?
— তৃতীয়? কেন হঠাৎ ওর নাম? সকলের নাম বলছি।
—সকলের নামই শুনব, আগে ওরটা শুনি। দুই বোনের পরে এসেছিল তো?
–ওর নাম ইনাফ ইজ এনাফ। সেই ইনাফ। আর বড় বোনের নাম বাপের আদরিণী, ফাদার্স ডার্লিং। মেজবোনের নাম খুশি, হ্যাপি।
একটুও অবাক হইনি। এইজন্যেই তিন নম্বরের মেয়ের নাম শুনতে চেয়েছিলুম। বাংলার গ্রামে যার নাম হয় আন্না (চাইনা), কিম্বা আর্নাকালী (আন্নাকালী) এখানে সে ইনাফ।
তোমার দেশ কি দক্ষিণ আফ্রিকা?
—হ্যাঁ, কিন্তু এখানে নয়, নাটালে ডারবানে। আমি জন্মেছি পিটারমারিৎসবর্গে। ছোট জায়গা। আমার মা বাবা এক বোন ওখানেই। আমি থাকি এখানে সোয়েটোতে যেখানে আমরা যাচ্ছি।
বাঃ, নন্দনা বলে ওঠে, –তোমার বাড়িটা আমাদের দেখিয়ো তো।
হেসে কুটোপাটি হয় সেফিসো।
—সে কি কথা? সোয়েটো যাবে নেলসন ম্যান্ডেলার বাড়ি দেখতে, উনি ম্যান্ডেলার বাড়িই দেখতে, বিশপ টুটুর বাড়ি দেখতে। সোফিসোর বাড়ি দেখতে কেউ কখনো সোয়েটো যায়? তা ছাড়া আমি তো আসলে ওখানকার লোক নই, আমার পড়াশুনো বড় হওয়া সব পিটার মারিৎসবর্গে। নাটাল প্রদেশে। ওখানে প্রচুর ভারতীয়েরও বাস। সাউথ আফ্রিকার সব চেয়ে বেশি ভারতীয়ের বাস সেখানে। কত ভারতীয় বাজার, দোকানপাট।
—আমি তো সেখানেও যাব, পিটারমারিৎসবর্গে। বলেই ফেলি।
মহা উৎসাহিত হয়ে সোফিসো বলে— সত্যি? কবে যাব?
—কালই। মহাত্মা গান্ধির নাম শুনেছ?
—জানি। তাঁর একটা সুন্দর লাঠি হাতে মূর্তি আছে আমাদের সিটি সেন্টারে, শহরের ঠিক কেন্দ্রে। ইন্ডিয়ার লোক। ম্যাণ্ডেলা তাঁর কথা বলেছেন। প্যাসিভ রেসিস্টেন্স।
আমরা মুগ্ধ সোফিসোর কথা শুনে। এতটা আশা করিনি।
সোয়েটোতে পৌঁছে প্রথমে সোফিসো আমাদের নিয়ে গেল ক্লিপটাউন বলে একটি পাড়াতে, একটি রাস্তার মোড়ে, এপারথেইডের মধ্যে ১৯৫৫ তে যেখানে ফ্রিডম চার্টার লিখিত হয়েছিল। একটি স্মৃতিস্তম্ভ আছে। ২০০৫-এ তার পঞ্চাশ বছর পূর্তির উৎসবের সময় খুব হৈ চৈ হয়েছিল। সোফিসো দৌড়ে গিয়ে আমাদের ফ্রিডম চার্টারের একটি কপি এনে দিল। আর দেখাল ছোট একটি গির্জে যেখানে বিপ্লবীরা, এই ওয়াল্টার সিসুলু, নেলসন ম্যাণ্ডেলারা নিয়মিত জড়ো হতেন ও স্বাধীনতার জল্পনা কল্পনা আলোচনা করতেন। মিটিং মিছিল মানা ছিল, সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ ছিল, এক ধর্মীয় সমাবেশ ছাড়া। তাই গির্জেই ভরসা। এই ফ্রিডম চার্টারের ভাষা সেই গির্জের মিটিংয়েই গোপনে তৈরি হয়েছিল। কিন্তু একদিন পুলিশ জেনে ফেলল এবং এসে গুলিও চালাল, গ্রেপ্তারও করল নেতাদের, গির্জের দেওয়ালে এখনও গুলির দাগ গর্ত হয়ে আছে। ওখানে গাড়ি পার্কিংয়ের সুবিধে নেই বলে আমরা আর নামি না, আমাদের দূর থেকে দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে, দূরে পার্ক করে এসে দেখে যাবার মতো সময় নেই। অগত্যা গাড়িতে বসে ফ্রিডম চার্টারটি উল্টে পাল্টে দেখছিলুম।
The Freedom Charter Adopted at The Congress of the People at Kliptown. On 26 June 1955.
(i) The People Shall Govern ( 2 ) All National Groups Shall Have Equal Rights (3) The People Shall Share in the Country’s Wealth ( 4 ) The Land Shall be Shared Among Those Who Work it(5)All Shall be Equal before The Law! (6) All Shall Enjoy Equal Human Rights (7) There Shall be Work and Security ( 8 ) The Door of Learning and Culture Shall be Opened (9) There Shall be Houses Security and Comfort (10) There Shall be Peace and Friendship
These freedoms we with fight for side by side, throught our lives, until we have won our liberty.
এই দশটি শপথের ভাষাই আমাদের খুবই পরিচিত মনে হচ্ছে না কি? পৃথিবীতে মানুষের এই লড়াই কি বন্ধ হয়েছে? ভারতবর্ষে কি এর প্রতিধ্বনি শুনিনি আমরা? লাঙ্গল যার জমি তার কি আমাদের অচেনা স্লোগান? আমাদের কি এখনও ইউনিফর্ম সিভিল কোড হয়েছে? হিন্দু মুসলমানের জন্যে ধর্মনিরপেক্ষ অভিন্ন আইন অন্তত সর্বক্ষেত্রে এখনও হয়নি। জাতিভেদের নোংরামি থামেনি, স্ত্রী-পুরুষের সামাজিক পরিস্থিতি এক নয়। নানা ক্ষেত্রে মানবাধিকারের লড়াই অবিশ্রান্ত চলেছে। গৃহহারাদের গৃহ নেই, চাষীদের জমির নিরাপত্তা নেই, শ্রমিকের কাজের নিরাপত্তা নেই, কোথাও যেন নিশ্চয়তা নেই, স্বাধীনতার বছর ষাট পরেও। দক্ষিণ আফ্রিকার সেই বর্ণবিদ্বেষী সরকারের তৈরি করা মৌলিক মানবতার অপমানসূচক আপারথেইডের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ১৯৫৫তে পরাধীন কালোমানুষের প্রতিবাদের ভাষা আজ ২০০৭-এও কেন আমাদের স্বাধীন ভারতের হৃদয়ের এত কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছে? তবে তো ডালমে কুছ কালা হ্যায়!
যাবার পথে সোফিসো আমাদের দেখাচ্ছিল সোয়েটো এককালে কুলিদের ঝোপড়িপট্টি ছিল বটে, কিন্তু এখন ধনীদের প্রাসাদে ছেয়ে গিয়েছে। ঝুপড়িও আছে, দারিদ্র্য নেই তো নয়, কিন্তু শহরের চেহারা বদলে গিয়েছে। এমনকী নাইটক্লাব, আজ পাব, কিছুরই অভাব নেই, বিদেশি কনসার্ট আসে। শুক্র শনি কেউ ঘুমোয় না এখানে। অবিকল মেলভিলের গল্প যে! পথে একটি স্কুলের সামনে দিয়ে যেতে গিয়ে দেখি ছুটির সময়, পিল পিল করে বাচ্চারা রেরুচ্ছে। শিশু কিশোর, ছেলে, মেয়ে—কিন্তু সকলেই কালো। একটাও সাদা মুখ দেখলুম না।
—এটা বুঝি কালোদের পাড়া?
—ঠিক তা নয়, এটা বড়লোকদের পাড়া বাড়িগুলো দেখছেন না? কি ফ্যান্সি?
–সে কি, তাহলে এই পাড়ায় শুধু কালো ছেলেমেয়ে কেন, এরা কি সবাই ধনী কালো? এত ধনী কালো পরিবার এখানে?
–নাঃ, এই সব বাড়ি সাদাদের প্রধানত। এটা সাদা পাড়া। এরা এ পাড়ার বাসিন্দা ঠিক
নয়। স্কুলে এসেছে।
—এখনও সাদা কালোদের আলাদা ইস্কুল? আলাদা আলাদা পাড়া? সে কি, তাহলে আপারথেইড উঠেছে কী করে?
—আইনত উঠে গিয়েছে। আলাদা ইস্কুল নেই। আলাদা পাড়াও নেই। তবে যে যার নিজের লোকের সঙ্গে স্বস্তিতে থাকে। অনেককালের অভ্যাস। সাদা কালো মিশিয়ে পাড়া আছে কিছু কিছু। উচ্চ মধ্যবিত্ত পাড়া। কিন্তু কেউ একসঙ্গে পড়ে না। কালো ছেলেরা ভর্তি হলে সাদারা ছেলেমেয়ে তুলে নিতে শুরু করে, অন্য স্কুলে দিয়ে দেয়। এমনি করেই সাদা পাড়াতে এই কালো স্কুল, সাদারা এখানে সন্তানদের আর পাঠায় না বলে কালোরাই ক্রমশ বেড়ে গিয়েছে সংখ্যায়।
একটু ইতস্তত করে সোফিসা আবার বলে,—আসলে আইনের নিয়মে তো মন চলে না? অভ্যাসের দোষ। তবে মিক্সড স্কুলও আছে, কালার্ড, এসিয়ান আর সামান্য কিছু সাদা ছাত্রছাত্রী একত্রে পড়ে এরকম হাতে গোনা কিছু স্কুলও ডারবানের কেপটাউনে আছে। বেশি নেই। যেখানে সবাই উচ্চবিত্ত এবং উদারপন্থী বাবা-মা, সেখানে আছে। দামি প্রাইভেট স্কুল। এমনিতে আমরা অবশ্য কালোদের স্কুলেই পড়েছি। সোফিসা বলে।
—আর ভারতীয়রা কোথায় পড়ে?
–কেন? ভারতীয়দের স্কুলে? অনেক ভাল ভাল স্কুল আছে ওদের। ভারতীয়রাই পড়ায় সেখানে। স্ট্যাণ্ডার্ড বেশ ভাল।
-সে কি? ভারতীয়দের আলাদা স্কুল? এখনও আলাদা পড়ে তারা? —এটা সঠিক জানি না। কিন্তু সম্ভবত তাই। খুব একটা বদল হয়েছে কি
এরপরে সোফিসো আমাদের নিয়ে গেল একদা কালোদের সেই বিখ্যাত ইস্কুলে, যেখান থেকে ছাত্রদের বিদ্রোহের সূত্রপাত। হেক্টর পিটারসন নামের ছেলেটি যেখানে পড়ত। বান্টু এডুকেশন বলে আপারথেইডের সময়ে একটি অসম সাম্প্রদায়িক শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছিল, কালো ছেলেদের শিক্ষার মাধ্যম হবে আফ্রিকান্স ভাষা। সাদাদের ইংরিজি। এতে কালোদের উন্নতির সুযোগ কমে যাচ্ছিল, জীবনে এগোনোর জন্য ইংরিজি জানা দরকার, শুধুই সাদারা ইংরিজি শিক্ষা পেত।
এক সময়ে কালো ছাত্ররা ক্ষেপে উঠল, তারাও ইংরিজি মাধ্যমে পড়বে, তারাও উঁচু মানের অংক শিখবে ইত্যাদি। একদিন ঠিক হল সব স্কুল থেকে ছাত্ররা বেরিয়ে এসে এক জায়গায় জড়ো হবে, এক বিশাল শান্তিপূর্ণ মিছিলে, আমরা আফ্রিকান্স চাই না, ইংরেজি মাধ্যমে পড়তে চাই এই মর্মে হাতে স্লোগান লেখা প্লাকার্ড নিয়ে হাঁটবে, তারা। ছাত্রনেতারা নির্দেশ দিল, সবাই সবচেয়ে ভাল জামাকাপড় পরে পরিচ্ছন্ন হয়ে সেজেগুজে ভদ্র সভ্য হয়ে আসবে, সেদিন দেখে যেন সম্ভ্রম হয়। শান্তিপূর্ণ মিছিল বলে বিশ্বাস হয়। ভাঙচুর গুণ্ডামি করতে এসেছে বলে না মনে হয়। কিন্তু পুলিশ এলে, সেজেগুজে প্লাকার্ড স্লোগান লিখে নিয়ে ছেলেদের মৌন মিছিল বেরুতেই, পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে আদেশ দিল। পুলিশের আদেশ মানল না ছেলেরা, তারা নিঃশব্দে নির্ভয়ে এগিয়ে চলল শান্তিপূর্ণ ভাবে। এবার পুলিশ গুলি চালালো, রবারের নয় সত্যিকারের বুলেট। লুটিয়ে পড়ল সবার আগে সামনে এগিয়ে যাওয়া সাহসী ছেলেটি, তারই নাম হেক্টর পিটারসন। ওই নাম কালোদের নাম নয়, সাদাদের আর কিছু কালার্ডদের। (এরা আমাদের অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের মতো। মিশ্র জাতি মিশ্র বর্ণ।) এদেশে প্রথমে যারা এসেছিল সেই হল্যাণ্ডের সাদারা তো ছিল স্বদেশ থেকে বিতাড়িত অপরাধী, সঙ্গে নারী ছিল না, তারা কালো নারীদের সঙ্গ করতে বাধ্য হয়েছিল, আর বাদামি সন্তানের জন্ম দিয়েছিল। পিতৃত্বের স্বীকৃতিতে বিদেশি ক্রিশ্চান নামও দিয়েছিল তাদের। গায়ের চামড়ার রং-এর দোষে সাদাদের সমান সম্মান না পেলেও, সাজে সেই কালার্ড শিশুদের অবস্থান কালোদের চেয়ে অনেক উন্নত ছিল। উচ্চশিক্ষার সুযোগ, ভদ্র চাকরির সুযোগ ছিল। হেক্টর পোষ্যপুত্র ছিল, তার বাবা ওকে পিটারসন পদবিটা দিয়েছিলেন কালার্ড ছেলেদের সুযোগগুলি যাতে সে পায়। হেক্টরের মৃত্যু থেকে শুরু হয়ে গেল ছাত্র বিপ্লবের অন্য এক সুর। সে সুরের রেশ চলেছিল ১৯৯৪ অবধি, যতদিন না আপারথেইডের অন্তিম মুহূর্ত এলো। সেদিনের কিশোর হেক্টরের ভাষা শহিদ হওয়া ব্যর্থ হয়নি।
১৯৭৬-এর আপারথেইডের অসম শিক্ষাপ্রণালী-বিরোধী আন্দোলনে সোয়েটো এবং অন্যান্য শ্রমিকপল্লীতে পুলিশের গুলিতে মোট প্রাণ দিয়েছিলেন অন্তত ৫৭৫ জন কালো মানুষ শিশু কিশোর নারী পুরুষ
ইস্কুলের পরে মোড়ের মাথায় দেওয়ালে একটি ফলক আছে, যেখানে লেখা আছে গুলি চালানোর কথা। সামনে কয়েকটি সিমেন্টের ছোট ছোট থামের মতন, তার ওপরে কিছু ইস্কুলের মেয়ে বসে গল্প করছে। আমি ক্যামেরা বের করতেই সরে গেল। ছবি তুলতে দেবে না।
–ঐ যে, সামনে ম্যাণ্ডেলার বাড়ি। ভিতরে যাবেন? ব্যবহৃত জিনিসপত্তর দিয়ে মিউজিয়ামের মতো করা আছে।
বিশাল এক বাড়ি দেখিয়ে বলে সোফিসো
-কেন? জাদুঘর এখনই কেন? তিনি তো স্বয়ং এখনও আছেন।
—এই বাড়িতে তো থাকেন না, জোহানেসবর্গে আছেন। তাহলে কী করবেন, যাবেন না? এর বিশপ টুটুর বাড়ি? সেটি দেখবেন কি?
—সবগুলোই দেখব, তীর্থস্থানের মতো, কিন্তু শুধু বাইরে থেকে মানুষগুলি ভিতরে থাকলে ভিতরে যেতে চাইতুম। শূন্য বাড়িতে কেন যাব? কার কাছে যাব?
–এই রাস্তাটার নাম মনে রাখবেন কিন্তু ভিলা কাজি স্ট্রিট, অরল্যাণ্ডো ওয়েস্ট। মনে থাকবে তো? অরল্যাণ্ডো ওয়েস্টে, ভিলা কাজি রাস্তা।
-কেন, হঠাৎ স্মৃতির পরীক্ষা কেন?
–বা রে? মনে রাখার মতো বিষয় নয়? পৃথিবীর আর কোনখানে এরকম একই রাস্তার ওপরে দুজনে নোবেল লরিয়েটের বসতবাড়ি আছে? নেলসন ম্যাণ্ডেলা আর বিশপ ডেসমণ্ড টুটু একই রাস্তার দু দিকে থাকেন। ঐ দেখুন? অসামান্য কাকতালীয় নয়?
তা বটে। প্রায় উল্টোদিকেই টুটুর বসতবাড়ি।
ম্যাণ্ডেলার বাড়িটি যেমন, টুটুর বাড়ি তেমন বিশাল বলে মনে হল না। তারপরে দেখলুম উইনির বাড়ি। বিশালতম, এবং প্রবল সিকিওরিটির ব্যবস্থা দোরগোড়ায়।
এই বাড়িতেই তাঁর সেই ফুটবলের টিমের সশস্ত্র ছেলেগুলি সব থাকত, যাদের মধ্যে চোদ্দ বছরের কিশোর স্টম্পি ছিল কনিষ্ঠতম। তাকে দলের ছেলেরা খুন করেছিল বলে উইনিকে খুনের দায়ে ধরা হয়েছিল। উইনির বিষয়টা আমার দেশে খুব দুর্বোধ্য আর রহস্যময় লাগত, এখন ট্রাজিক লাগছে।
এই জোহানেসবর্গে একদা গান্ধিজিও বসবাস করেছেন সপরিবারে। কোর্টে লড়াই করেছেন, রাস্তায় পুলিশ-এর জুলুম বরদাস্ত করেছেন, মস্তানদের হাতে মার খেয়েছেন, ভারতীয়দের টিপছাপ নিয়ে জবরদস্তি রেজিস্ট্রেশন করানোর চরম অবমাননাসূচক সরকারি বিলের বিরোধিতা করে আন্দোলন শুরু করেছেন, বিল পাস হয়ে যাবার পরেও বিলেতে অবধি দৌড়াদৌড়ি করে সেই কালা আইন শেষ অবধি রুখেছেন, প্যাসিভ রেসিস্ট্যান্স শব্দটির জন্ম দিয়েছেন, এখানে, ও ভারতীয়দের আত্মসম্মান -সচেতনতার রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্মও এখানে। এখানে তাঁর চমৎকার বাড়িঘর ছিল, আটখানা শোবার ঘর, বাগান দিয়ে ঘেরা, সামনে সবুজ লন, উচ্চমধ্যবিত্ত পাড়াতে পেয়েছিলেন বাসা, ভারতীয় হয়েও। সেখানে সপরিবারে, কিছু দিশি ও বিদেশি আশ্রিত বন্ধু সমেত আশ্রমিকেরা জীবনযাপন করতেন। ব্যারিস্টারের এমন নিরহংকার গৃহস্থালি কেউ দেখেনি। কার্পেট ছিল না, পর্দা নয়, রোদ্দুর আটকাতে হলুদ খড়খড়ি ছিল শুধু। আসবাবপত্র যেটুকু না হলে নয়, সেইটুকুই। ডারবানে আর জোহানেসবর্গে তাঁর ছুটোছুটির জীবন কেটেছিল। অনেকদিন। কিন্তু টুরিস্টদের দ্রষ্টব্যস্থলের মধ্যে সেসব বাড়ি পড়ে না। এসেছি মাত্র একটি দিনের জন্য, সময় হাতে নেই, থাকলে আমি ঠিকই খুঁজে বের করে নিতুম গান্ধিজির স্মৃতি জড়ানো জোহানেসবর্গ। এ যাত্রায় প্রিটোরিয়া হল না। এবার শুধু ডারবানের স্মারকচিহ্নগুলির দিকেই নজর রেখেছি। কাল সেখানে যাব। যদিও নন্দনাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া গেল না, এজন্য মা মেয়ে দুজনেরই মন খারাপ, ওর শুটিং শুরু কাল থেকেই। কিন্তু জোহানেসবর্গে এসে গান্ধিকে মনে না পড়াও তো সম্ভব নয়। এই আমাদের দেখা দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম শহর। আর দক্ষিণ আফ্রিকা আমাকে চিনিয়েছেন, ম্যাণ্ডেলা আর নাদিন গর্ডিমারের ঢের আগে, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি। এই যে সোয়েটোতে কালো স্কুল বালকদের ১৯৭৬-এর শান্তিপূর্ণ শক্তিপ্রদর্শন, প্রাণ দেব কিন্তু মান দেব না, এই প্যাসিভ রেসিস্টান্স, ম্যাণ্ডেলার কুড়িয়ে নেওয়া এই আত্মশক্তির নীতি কার উপহার দক্ষিণ আফ্রিকাকে? ম্যাণ্ডেলা তাঁর বিখ্যাত আত্মজীবনীতে স্বীকার করেছেন, গান্ধির নীতি গ্রহণ করা ভিন্ন আর কোনও পন্থা ছিল না তাঁদের সামনে। ১৯৯৪-এ স্বাধীন হয়েছে আফ্রিকা, ম্যাণ্ডেলা ছিলেন প্রথম প্রেসিডেন্ট, অদ্যাবধি কিন্তু কোনও গান্ধি মিউজিয়াম গড়ে ওঠেনি এখানে অবশ্য আপারথেইড মিউজিয়ামে গান্ধি বিষয়ক কিছু আছে কিনা জানি না, সেখানে যাইনি, তবে না থাকাই স্বাভাবিক।
আমাদের তার পরের গন্তব্য হেক্টর পিটারসন মিউজিয়াম। আপারথেইড মিউজিয়ামেও নিয়ে যেতে ইচ্ছে ছিল সোফিসোর, কিন্তু আমাদের নাদিন গার্ডিমারের বক্তৃতার জন্য তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। দুটো মিউজিয়াম সময়ে কুলোবে না। আমরা এটাই বেছে নিই। হেক্টর পিটারসন মিউজিয়ামের সামনে একটি সুন্দর স্মৃতিস্তম্ভ, একটি ফোটোগ্রাফ বড় করে বাঁধানো তাতে হেক্টরকে কোলে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, বাচ্চা ছেলে সদ্য কিশোর। ফলকে লেখা আছে সেদিনের ইতিহাস ও শ্রদ্ধা ১৬ জুন ১৯৭৬।
মিউজিয়ামের ভিতরে প্রচুর ছবি, সোয়েটোর কুলি বস্তির পত্তনের ইতিহাস, ছাত্র রাজনীতির ইতিহাস। তারই সঙ্গে জড়িয়ে আছে দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস। ছাত্র বিপ্লবের, মিছিলের অনেক ছবি, প্লাকার্ডে স্লোগান লেখা : বেশ রাগী স্লোগান, টু হেল উইথ আফ্রিকাআনস ( Afrikaans )! আফ্রিকাআন্স মাস্ট বি অ্যাবলিশড!’ আফ্রিকাআন্স আফ্রিকাবাসীদের বহুবচন নয়, আফ্রিকাআন্স একটি ভাষা, ডাচ ও জার্মানির মিশ্রণে তৈরি, কালো আফ্রিকার উপরে সাদা প্রভুত্বের ভাষা। আপারথেইডের কর্তাদের ভাষা। ঐ ভাষার দ্বারা কালো ছাত্ররা শৃঙ্খলিত বোধ করছিল। ঐ ভাষার সঙ্গে জড়িয়ে আছে দক্ষিণ আফ্রিকার দাসত্বের ইতিহাস। আর দক্ষিণ অফ্রিকার বাইরে ঐ ভাষার কোনও অস্তিত্ব নেই। তাই তারা চেয়েছিল শিক্ষার সমতা, চেয়েছিল সাদা ছাত্রদের মতোই আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরিজির মাধ্যমে শিক্ষা তাদের জন্যও চালু হোক। মিউজিয়ামের হিসেব অনুযায়ী প্রতি সাদা ছাত্রের জন্য সরকার যেকানে ৬৪৪র্যাণ্ড খরচ করতেন, তখন কালো হলে ছাত্র প্রতি বরাদ্দ শুধু ৪২ র্যাণ্ড। অবিশ্বাস্য? না, এ তো আপারথেইডের দক্ষিণ আফ্রিকার চেহারা। শুধু তাই? স্কুলে সাদা বাচ্চারা পাঠ্যপুস্তক পেত বিনামূল্যে, আর কালো ছাত্র, যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, তাদের কিন্তু পাঠ্য বই পয়সা দিয়ে কিনতে হত। স্কুল ফ্রি দিত না। মিছিলের ছবিতে আরো কত প্লাকার্ড, একটি বলছে, ‘উই আর নট ফাইটিং, ডু নট শূট, জাস্ট রিলিজ আওয়ার ফেলো স্টুডেন্টস!’ তাতেও গুলি চলেছিল।
প্রচণ্ড অবাক লেগেছিল দু হপ্তা কেপটাউন থেকে বেরিয়ে ফরাসিদের প্রতিষ্ঠিত ওয়াইন কান্ট্রি ঘুরতে ঘুরতে পার্ল শহরের এক টিলার চূড়োতে যখন আফ্রিকাআন্স ভাষার মাহাত্ম্য স্মরণে একটি সম্মানস্তম্ভ দেখলুম। যে ভাষার জন্য এত কাণ্ড এতগুলি প্রাণ গিয়েছে তার জন্যে বুঝি সম্মানের মনুমেন্ট গড়তে হয়? আমার কাছাড়ের, আর বাংলাদেশের ভাষা শহিদদের মনে পড়ে যাচ্ছিল। ঢাকাতে কি উর্দুর জন্য সম্মানসূচক স্মৃতিস্তম্ভ গড়া যেত? কিংবা করিমগঞ্জে অসমিয়ার জন্য? গড়াটা কি মানবিক হত?
হেক্টর পিটারসেনে অনেক অল্পবয়সী বিপ্লবীদের ছবি আছে, এখানেও গান্ধি জিন্নাদের মতোই আইনজীবী তরুণের দল স্বাধীনতার জন্যে সর্বান্তঃকরণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাঁদেরই ছবি আছে। তাঁদের মধ্যে জ্বলজ্বল করছে তরুণ নেলসন ম্যান্ডেলা, ওয়াল্টার সিসুলুদের ছবি। আলাদা করে স্মরণযোগ্য একটি কথা এখানে বলতে চাই, জাদুঘরে গিয়ে যেটি আমার যারপরনাই আকর্ষণীয় লাগল। দেশের বিপ্লবের ও স্বাধীনতার ইতিহাসে মহানায়কদের স্ত্রীদের বিশিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা এখানে আলাদা করে সসম্ভ্রমে উল্লিখিত। সিসুলুর স্ত্রী আলবের্টিনা আর ম্যাণ্ডেলার স্ত্রী উইনির মাহাত্ম্যপূর্ণ অবদানের প্রতি বর্তমান সরকারের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি রয়েছে সেখানে। আমাদের দেশের ইতিহাসে কস্তুরবার কিংবা কমলা নেহরুর আত্মত্যাগের উল্লেখ এভাবে থাকে কি?
—উইনিকে তোমার কেমন লাগে? বাড়ি ফেরার পথে প্রশ্ন করলুম সোফিসাকে।
সোফিসো নির্দ্বিধায় উত্তর দিল—উইনি ধৈর্য ধরে ২৫ বছর একটানা মানুষের মধ্যে আন্দোলনের আগুন জীইয়ে না রাখলে, রাশ টেনে ধরে না থাকলে কি আজ স্বাধীনতা আসত? বড় মানুষরা তো জেলে বন্ধ ছিলেন। দেশের মানুষ যে আপারথেইড সরকারের অপচেষ্টা ব্যর্থ করেছে, সে তো অনেকখানি ওরই চেষ্টায়, এক উইনির গোপন গণ-আন্দোলনের ফলে। পরে সে যাই করুক। তাতে আগের ভাল কাজটা তো মুছে যায় না?
উইটস • নোবেল • বালক নোবেল বালিকার নিভৃত আলাপন
সোয়েটো থেকে ফিরে তখনও আমরা গাড়ি থেকে নামিনি, এক ভদ্রলোক এসে জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালেন। অনেকদিনের চেনার হাসি হেসে বললেন, ‘নবনীতা? আমি ম্যালকম। পিপার স্বামী। তোমাকে আর নন্দনাকে ইউনিভার্সিটিতে নিয়ে যেতে এসেছি, নাদিন গর্ডিমার আর অমর্ত্যর আলোচনাসভাতে। সেখান থেকে নিয়ে যাব ডিনারে। তোমাদের জন্য আমি এই রাস্তায় মাত্র একটা ঘণ্টা অপেক্ষা করছি।’
লজ্জা পেয়ে আর বাড়ির ভিতরে না ঢুকে, এ গাড়ি থেকেই ঝাঁপ দিয়ে ও গাড়িতে উঠে পড়ি। সারাদিনের ঘোরাঘুরির পরে যেমন ছিলুম তেমনি ছুটলুম দুজনে, উপায় কি? মা-মেয়েতে একটু যে মাঞ্জা মারব তার সুযোগ হল না। নন্দনা তো সহজ সুন্দরী। আমিও ভেবে নিলুম আমিও বেশ তা–ই। ভাবতে ক্ষতি কী?
বিরাট ঝামেলা হল সিকিওরিটির কবল থেকে গাড়ির ছাড়া পেতে। অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলল। যদিও প্রফেসর ম্যালকম স্টাইন এখানেই পড়িয়েছেন এতদিন। এখন বিখ্যাত মার্কেট থিয়েটারের আর্টিস্টিক ডিরেক্টর। তাঁর স্ত্রী স্বয়ং এই সভার আয়োজক। তবুও। এই না হলে পুলিশ? তায় দক্ষিণ আফ্রিকার!
অসম্ভব ভীড়, হল উপচে গিয়েছে। ছটার সময়ে হলের দরজাগুলি বন্ধ। আজ সেই মর্মে বাইরে নোটিশ লটকে দেওয়া হয়েছে। খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে মঞ্চ। একদিকে একটি ভারতীয় কারুকার্যখচিত মস্ত কাঠের দরজা, তোরণের মতো। তার পাশে বিশাল দুটি ঝকঝকে পেতলের টবে দুটি আস্ত মস্ত কলাপাতা হেলিয়ে রাখা হয়েছে এমন করে, দেখেই সরস্বতীপুজোর দোয়াত কলমের কথা মনে পড়ল আমার। যেন সোনার দোয়াতে হাঁসের পাখার কলম। তার এপাশে মঞ্চের মাঝখানে কয়েকটি আরামকেদারা পাতা, আড্ডা দিতে অসুবিধে হবার কথা নয়।
কিন্তু তোরণ রইল পড়ে, মঞ্চের অন্যদিক থেকে নাটকবিহীনভাবে নায়ক-নায়িকার প্রবেশ, অশীতিপর নাদিন কিন্তু এখনও সুন্দরী এবং চটপটে আছেন, সেই দিল্লিতে যেমন দেখেছিলুম প্রায় তেমনই। তবে এতদিনে একটু বয়সের হাওয়া লেগেছে। নিজের শহরে তিনি অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ, একটু সম্রাজ্ঞীর মতো হাব-ভাব, যদিও ছোট্টোখাট্টো। অমর্ত্যর সঙ্গে এই সপ্তাহে তিনটি প্রোগ্রাম, উনি নাকি চারটি সম্মিলন চেয়েছিলেন, কিন্তু কেপটাউনের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস চ্যান্সেলার স্পেশাল অ্যাড্রেস না কী যেন এক ভাষণ দেবার আছে অমর্ত্যর। তাই তাঁর সময়াভাব। অগত্যা মাত্র তিনবারেই ক্ষান্ত হতে হল নাদিনকে। অমর্ত্যকে যেহেতু তাঁর খুব পছন্দ, তাই দুর্ভাগ্যবশত কোনও ব্যাপারেই তাঁদের তেমন অমত হচ্ছে না, আর সেই কারণে হায়, বিতর্ক জমছে না, এই বলে প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিয়ে নাদিন তার বক্তব্য শুরু করলেন। অল্পবয়সী অর্থমন্ত্রী মশাইকেও ধমকে বললেন, তুমিও তো দেখছি অমর্ত্যের সব মতেই মত দিয়ে চলেছ, ট্রেভর, আজ কিছু অমত শোনাও?
অমতের তেমন প্রাবল্য না হলেও সব মিলিয়ে আলোচনা জমজমাট হল, রঙ্গ রসিকতাতে বক্তারা কেউ কম যান না। দুই নোবেল বালক নোবেল বালিকা-র সঙ্গে মন্ত্রীমশাই ছাড়াও যে মাননীয় জজসাহেব মঞ্চে ছিলেন, তাঁর সুরসিক ও মেধা উজ্জল মন্তব্যগুলিও যারপরনাই চমকদার। ট্রেভর ম্যানুয়েল ভারত বিষয়ে খুব ভাল খবর রাখেন দেখলুম। নন্দীগ্রাম সিঙ্গুর বিষয়েও ঠিকঠাক আপ-টু -ডেট অনুপুঙ্খ জানেন দেখে আমি কিঞ্চিত চমৎকৃত না হয়েই পারিনি। কেননা আমি দেখেছি, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের লোকেদের মধ্যেও এই বিষয়ে অজ্ঞতার ও নিরুৎসাহের শেষ নেই। অমর্ত্যের আগামিকালকের বক্তৃতার বিষয়টি সোজা নয়। সোসাল জাস্টিস ইন সাউথ আফ্রিকা টুডে। কোনও বিদেশির পক্ষে দুঃসাহসী বিষয়।
কিন্তু আমাদের শোনা হবে না। আজকের আলোচনা অনেকটা ছড়ানো, মূলত অমর্ত্যর গতকালকের নাদিন গর্ডিমার বক্তৃতার ওপরেই। দারিদ্র্য ও হিংসা নিয়ে প্রধানত কথা হচ্ছিল। উপস্থিত সকলেই গতকালও শ্রোতা ছিলেন বলে বোঝা গেল। অমর্ত্য কোনও প্রসঙ্গে কলকাতার উল্লেখ করে বললেন আমার নিজের শহরে দারিদ্র্য খুব বেশি হলেও ক্রাইম তার তুলনায় অনেক কম, অথচ দিল্লিতে দারিদ্র্য কম, অপরাধ বেশি। অর্থাৎ সর্বদা দারিদ্র্যের সঙ্গে হিংসা ও অপরাধকে জড়িয়ে ফেলা ঠিক নয়। সেটি অতি সরল হিসেব। হিংসার পিছনে আরো অনেক গূঢ় ও জটিল কার্যকারণ কাজ করে। আলোচনা দারুণ জনপ্রিয় হল, প্রত্যেক বক্তারই বক্তব্য পরিচ্ছন্ন ও ঝকঝকে, উপরন্তু চারজনেরই অসাধারণ কৌতুকের প্রতিভা থাকায় শ্রোতাদের মন ভরে গেল।
মূল আলোচনার পর শ্রোতাদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর। এক মহিলা অর্থমন্ত্রীকে প্রশ্ন করলেন—’বইএর ওপরে সেলট্যাক্স থাকা কি উচিত? এতে বই কেনার ও বই পড়ার উৎসাহ কি কমে যায় না?
মন্ত্রী তোতলাচ্ছেন দেখে নাদিন করুণাপরবশ হয়ে তাঁর সহায়তায় এগিয়ে গেলেন। ‘অন্যান্য সব জিনিসের মতো বইও বিক্রি হয়, বইও পণ্যদ্রব্য। পণ্যের উপর বিক্রয়কর থাকে, বই-এর উপরে থাকবে না কেন? আর বই সবাই পড়ে না, পড়লেও কেনে না। যারা কেনবার তারা ভালবেসে কেনে। নেশায় কেনে। তারা বিক্রয়কর দিয়েও কিনবেন। বিক্রয়কর থাকুক, আমি মনে করি না এতে বই বিক্রি কমবে।’ অর্থনীতিবিদ সেন মশাই কিন্তু এবারে অবশেষে নাদিনের বিপক্ষে গেলেন, তিনি বললেন, ‘আমি মনে করি বই অন্যান্য পণ্য থেকে আলাদা, মানুষকে বই পড়ায় সরকারের উৎসাহ দেওয়া উচিত, যারা ভালবেসে বই কেনেন তাদের সেজন্য শাস্তি দেওয়া উচিত নয় শুল্ক বসিয়ে! না, বইতে সেলট্যাক্সের আমি বিরুদ্ধে।
আবার হাততালিতে ঘর ফাটল, এখানে সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের মানুষ, ছাত্র-মাস্টার, সবাই তো বই-কিনিয়ে, বই পড়ুয়ার দল। নাদিনের হৃদয়হীন খটখটে জবাবে তাঁরা খুশি হননি। হকচকিয়ে চুপ করে গিয়েছিলেন। সম্ভ্রমবশত আপত্তি জানাননি। এতক্ষণে খুশি হলেন।
আলোচনাতে বেশ পরিতৃপ্ত হয়ে সবাই বেরুলেন, ভাবখানা এই, আরো কিছুক্ষণ চললে ভাল হত। কিন্তু আসলে ঠিক সময়ে থামাটাও একটা অনুষ্ঠানের সার্থকতার জন্য জরুরি। ‘ওফ, বা-ব্বাঃ! আরো একঘন্টা আগে থামলে ভাল হত,’ শ্রোতাদের এমন যাতে কক্ষনো না মনে হয়। সেদিক থেকে আদর্শ টাইমিং হয়েছিল।
উটপাখির বড়া • কুমিরের মাংস ভাজা।
এর পরে নাদিনের সঙ্গে নৈশভোজে গেলুম অমর্ত্য ও বাকি আলোচক দুজন সমেত আমরা জনা দশ বারো, নন্দনা ও নাদিন ছাড়া সকলেই অধ্যাপক। রেস্তোরাঁটি মার্কেট থিয়েটারের লাগোয়া, মোমবাতির আধো অন্ধকারে, লম্বা টেবিলে বসেছি সবাই, আমার বিপরীতে নাদিনকে বসিয়েছেন ওরা, যাতে আমরা দুই লেখকে কথাবার্তা বলতে পারি। কিন্তু চারিদিকে খুব শব্দ হচ্ছিল, কিছু বাজনার, কিছু বাক্যের আর নাদিন খুব মৃদু কণ্ঠে কথা কন, যদিও কথাগুলি খুব মৃদু চরিত্রের নয়, বেশ কঠিন কঠিন কথাই বলেন। কথোপকথন সহজ ছিল না টেবিলের এপাশ থেকে ওপাশে। এক সময়ে কথার পিঠে কথার মধ্যে নাদিন গলায় জোর দিয়ে বলে উঠলেন, ‘যদিও আমি আমার নিজের লিঙ্গের বিরুদ্ধে কথা বলছি, তবুও বলব পুরুষের মন নারীর চেয়ে উদার এবং তাদের সূক্ষ্ম বোধ আছে, নারীরা অনেক নীচ এবং স্থূল, তারা সূক্ষ্ম জিনিস বোঝে না।’ স্তব্ধতা নেমে এল বটে, কিন্তু টেবিলের কেউ তাঁর বাক্যের প্রতিবাদ করলেন না। আমিও না। অত বয়সে মানুষের মনের জটগুলো আর বিতর্ক দিয়ে উন্মোচিত করা যাবে না।
সে যাই হোক, খাওয়াটা খুব উৎসাহব্যঞ্জক, কুমিরের মাংস ভাজা, উটপাখির মাংসের বড়া, কাঁকড়ার চচ্চড়ি, ঝিনুকের মাংসের চাটনি, আফ্রিকান মশলার মাংসের ভুনি খিচুড়ি! আরো কত কী। নন্দনা আমাকে কষ্ট করে উঠতে দেয়নি, নিজে গিয়ে সব অসাধারণ আফ্রিকান পদগুলি বেছে বেছে তার অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় মা জননীর জন্যে প্লেটে তুলে এনেছে। তার আগে অবশ্য হাঁপানি নিরোধক অ্যান্টিঅ্যান বড়ি খাইয়ে দিয়েছে। স্বাধীনচেতা নাদিন অপরের সাহায্য নিলেন না, উঠে গেলেন নিজের জন্য নিজে দেখে শুনে খাবার বেছে নিতে। বললেন, অন্য কেউ বেছে এনে দিলে ওঁর পছন্দ হয় না। মিষ্টান্নের বেলাতেও উঠে গেলেন, মালবা পুডিং নামক বিখ্যাত আফ্রিকান মিষ্টান্নটি খেতে উনি ভালবাসেন, সেটি আছে কিনা দেখতে। মালবা অনেকটা ক্রিসমাস পুডিং-এর মতো, আরো হাল্কা। ভ্যানিলা আইসক্রিম সহযোগে মহানন্দে সেটি গলাধঃকরণ করলেন নাদিন। আমার দেখেও ভাল লাগছিল, জীবনের প্রতি তাঁর এতটা উৎসাহ, এত আসক্তি, যৌবনের থেকে কম কিসের?
(আমি সেদিন মিষ্টি খাইনি, কিন্তু পরে এই মালবা পুডিং খেয়েছি কেপটাউনের মাম্মা আফ্রিকা রেস্তোরাঁতে।) খাবার টেবিলে আড্ডা জমেছিল মন্দ না, আশেপাশে যে অধ্যাপকেরা ছিলেন তাঁরা খুব মিশুকে, আর নাদিনও আড্ডা দিতে ভালবাসেন। যদিও মেয়েদের বিষয়ে ঐ মন্তব্যের পরে আমার আর তেমন ভাব হয়নি ওঁর সঙ্গে। একটুতেই আমার মনের সুর কেটে যায়। এটা আমার চরিত্রের ত্রুটি। ওঁর একটা ছোট গল্পের বই আমার কাছে ছিল, জাম্প। সেটি সই করে দিলেন। আমি তাতে আমার নামটা লিখতে বলিনি, উনি তো আমাকে দেননি বইটা?
সেদিন রাত্রে ফিরে এসেই দুজনে নেতিয়ে পড়ি ঘুমে। কাল ভোরের বেলাতে আবার বেরুনো। গোপালকৃষ্ণ গান্ধি বলেছিলেন হাতে কম সময় থাকলেও সোয়েটো আর গর্ডিমার এই দুটি আমার জোহানেসবর্গে অবশ্য দ্রষ্টব্য। দুই-ই হল। একটাই দুঃখ, জিজ্ঞাসার সঙ্গে আরো সময় কাটানো গেল না। ওর সঙ্গে প্রশান্ত আর আলোক নামে দুটি কলকাতার ছেলে ছিল। তিনজনেই টাটা কন্সালটেন্সিতে কাজ করে। আমার পুষ্যি কন্যে শ্রাবস্তীই এদের ফিট করেছে ফোনে, মা আর ছোড়দির জোবর্গের দেখাশোনার জন্য। শ্রাবস্তীর বন্ধু অরিজিতের সহকর্মী এরা সবাই। কিন্তু আমরা তো থাকছি না। ওরা বারবার বলল কেপটাউনে ওদের বন্ধুবান্ধব আছে, গিয়ে ফোন করলে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবে। আর যেন ফেরার পথে দুটো দিন জোবর্গে অতি অবশ্যই জিজ্ঞাসার সঙ্গে কাটিয়ে যাই। জোহানেসবর্গে ঘোরাঘুরির বহুত বাকি রয়েছে। আমারও সেটা ইচ্ছে, কিন্তু দেখি কীভাবে কী হয়।
ও ভাই, ডারবানের প্লেন কোনটা?
তারপরের দিন ভোরে বেরিয়ে পড়ি এলসার সঙ্গে। পুরনো জোহানেসবর্গের ভিতর দিয়ে দেখাতে দেখাতে নিয়ে যায় এলসা। ওর শহর নিয়ে ও খুব গর্বিত। এলসা একদার রাজত্বকারী বার্গার পরিবারের মেয়ে। নীল চোখ, সোনালি চুল, দীর্ঘকায়। নাদিনও বার্গারের কন্যা, এই নামেই তাঁর আত্মজীবনী আছে। এলসার সঙ্গে বর্ণবিদ্বেষের বিষয়ে বাক্যালাপ করা হয়ে ওঠেনি। এলসা দেখাচ্ছিল, ঐ যে সোনার খনি ছিল ওখানে, তারই স্মারক ঐ টাওয়ার দু-টা। এখানে হিরের খনিও পাওয়া গিয়েছিল, ত্রান্সভালে প্রচুর কুলিদের আনা হয়েছিল বাইরে থেকে খেত খামারের কাজের জন্যে। কেননা স্থানীয় কালোরা সেদিকে বিশেষ কাজের নয়। সেই বাইরের কুলিদের উত্তরপুরুষেরাই এদেশে এখনকার মধ্যবিত্ত—এশিয়ান বাসিন্দা, চিন, মালয়, ভারতবর্ষের লোকেরা। খনির কাজে অবশ্য ওরা ছাড়া স্থানীয় আফ্রিকান কুলিরাও ছিল জোহানেস নামের দুজন ইউরোপীয় লোক এখানে সোনার খনির খোঁজে এসেছিল, তাদের দুজনের নাম মিলিয়েই এই জোহানেসবর্গ নাম হয়েছিল।
—ওরা যখন আসেনি তখনও তো এই জায়গাটা ছিল? কী নাম ছিল তখন এই জায়গার?
—সে আফ্রিকান ট্রাইবাল নাম-টাম কোনও ছিল হয়তো। কেউ জানে না। ঐ দ্যাখো এই যে পুরনো গির্জে, ঐ যে পাশেই পুরনো সিনাগগ। কী সুন্দর, না? কী সম্ভ্রান্ত। এখন তো অন্য কাজে ব্যবহৃত হয়, এই সিনাগগে আর পুজো হয় না। এখানে কোনও জলাশয় নেই, কোনও নদীতীর নেই, কোনও সাগর সৈকত নেই, ব্যবসায়ীদের শহর এই জোহানেসবর্গ, জলের কাছে যাবার উপয় নেই। তবু প্রচুর সবুজ গাছপালা, সবই মানুষের লাগানো শ্যামলিমা। মি কাসা সু কাসা নামের সুন্দর অতিথিশালাটি ছেড়ে আসতে ইচ্ছে করছিল না। ইংরিজিতে কোজি বলে একটা শব্দ আছে, জানি না ঠিক বাংলাতে কীভাবে বলব। ওম্? কবোষ্ণ? এয়ারপোর্টে এসে মা মেয়ে আলাদা, একই সময়ে ছাড়ছে দুটি উড়োজাহাজ। মেয়েটা উড়ে গেল কেপটাউনে আমি ডারবানে।
আমি কিন্তু এ যাত্রায় ডারবানে না-ও যেতে পারতুম। একটি চমৎকার লিফট করা আছে যাতে সব কজন চক্র চেয়ারের আরোহীদের বসিয়ে একসঙ্গে প্লেনে তুলে দেওয়া ও নামিয়ে আনা হয়। দেশের মতো বল হরি হরি বোল চেয়ার-টাকে কাঁধে তোল হেঁইয়ো হেঁইয়ো করে হুইলচেয়ারটা প্লেনে তোলে না। সেদিন পড়লুম দিল্লিতে এই করতে গিয়ে একজন ভগ্নপদ অসুস্থ আরোহীকে ফেলেও দিয়েছেন বাহকেরা। বেশ আনন্দে আমরা চারজনে টারম্যাকের ওপরে লিফটের গাড়িতে বসে আছি তো বসেই আছি। একটি প্লেন সামনে অপেক্ষমান। একটু বোর হচ্ছি সবাই। আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ যিনি করছেন সেই যুবকটির অসীম এনার্জি এবং খোশমেজাজ। আপনমনে গান গাইছেন, সঙ্গে অল্পস্বল্প নৃত্যভঙ্গিমাও করছেন আমাদের মনোরঞ্জনের আশায়, খুবই হাসিখুশি ছেলে। আমাদের অস্থিরতার আঁচ পেয়ে তিনি বললেন, রাই ধৈর্যম্ রহু ধৈর্যম্, প্লেনটা এক্ষুনি নেমেছে, এখন যাত্রী বেরুবে, তার পরে ধোয়া মোছা, তার পরে তোমাদের আরোহণের পালা। আমাদের মধ্যে যিনি বৃদ্ধাতমা তিনি সমানে গুনগুন করে কী একটা অভিযোগের সুর সর্বক্ষণ ভেঁজে চলেছেন।
—কী গ্রাম্মা কী বলছ? হাস্যবদনে ছেলেটি গান থামিয়ে বলে। ঠাম্মা বললেন,—বলছি ঐটা কোথায় যাচ্ছে, ঐ যে, ঐ প্লেনটা?
-কেন? ডারবানে!
–না, ডারবানে নয়। আমি অনেক বছর ধরে ডারবানে যাচ্ছি। আমি জানি ডারবানের প্লেন এখানে থামে না, অন্য ঘাটে লাগে। আমি জানি। এই বে-টা ডারবানের বে নয়। তুমিই জান না বাছা। আগে তুমি খবর নাও ওটা কোথায় যাচ্ছে। আমি কিছুতেই ওতে চড়ব না আমাকে ভিতরে নামিয়ে দিয়ে এস। শুনে হেসে কুটিপাটি হয় তরুণ,—ও গ্রাম্মা তাই কখনো হয়? ড্রাইভারের তো এটাই কাজ। ও কি তোমাদের ভুল প্লেনে তুলতে পারে? কী বলছ ঠাম্মা? ভবি ভোলার নয়। বৃদ্ধা শুনবেন না।—তুমি ফোনে অফিসে এক্ষুনি জিজ্ঞেস করো ঐ প্লেনটা কোথায় যাবে। আমি জানতে চাই।
ওকে ভোলাবার জন্য কুলকুলিয়ে হাসতে হাসতে ছেলেটি ফোন করে,— হে বস, গ্রাম্মা হিয়ার ওয়ান্টস টু নো অমুক নম্বরের বে থেকে প্লেনটা এখন কোথায় যাচ্ছে? ডারবানে তো?
তারপরেই তার কালো মুখে ঘন কালো ছায়া ঘনিয়ে আসে। গান বন্ধ হয়ে যায়। দোর খুলে নেমে যায় সে ড্রাইভারের সঙ্গে ঝগড়া করতে। ফিরে এসে খুব শান্ত লজ্জিত ভাবে বলে, ইউ ওয়ের রাইট গ্রাম্মা, গ্রাম্মাস আর অলওয়েস রাইট। উই হ্যাভ টু গো টু এনাদার বে ফর ইয়োর প্লেন। নো প্যানিক, প্লেন্টি অফ টাইম, ইয়োর প্লেন জাস্ট ল্যাণ্ডেড।
অতএব সেই অভিজ্ঞ মহিলার তীক্ষ্ণ অনুপুঙ্খের দৃষ্টির গুণে আমরা অজ্ঞাতভ্রমণের সুখ থেকে বঞ্চিত হলুম। যথাকালে ডারবানের প্লেন আমাদের বুকে নিয়ে উড়ল। এমনও যে হতে পারে সেটা জেনে বুক শুকিয়ে গেল। চারজন কিঞ্চিৎ প্রতিবন্ধী মহিলা আর একটু হলেই ভুল গন্তব্যে রওনা হতেন, যদি ঐ টরটরি বৃদ্ধার তীক্ষ্ণ নজরে না পড়ত। এদেশের এই বদনামটি আছে। লেইড ব্যাক। একটু গয়ং গচ্ছ, একটু এলিয়ে থাকা স্বভাব, সারাক্ষণ অতটা রিল্যাক্সড থাকলে কি কাজকর্ম গুছিয়ে করা যায়? এখানে এসে বুঝলুম একটু টেনশন থাকা ভাল।
নন্দনা অবশ্য পরে এসব ভয়ংকর খবর শুনে ভয় পাবার বদলে হেসে কুটিপাটি হল, তার পরে বলল অন্য প্লেনটাতে চড়লেও তো ভালই হত মা, আরো একটা শহরে ফ্রি বেড়ানো হয়ে যেত তোমার, প্লাস খানিকটা অ্যাডভেঞ্চার, ‘ফোর উইমেন অন দ্য রং ফ্লাইট’ গল্প লিখে ফেলতে পারতে।
প্লেনে ঠিকঠাক উঠে আরেক চমক। আমার পাশে কাকে পেলুম? আরে, সুনাম যে! বিশ্ব বড়ই ছোট হয়ে এসেছে। সুনাম আমাদের দিল্লির পুরনো বন্ধু বিদ্যুৎ সরকারের ছেলে। সে সামনের সিটে বসেছিল। হঠাৎ তার আবাল্য চেনা মার্কা মারা খসখসে অপরূপ কণ্ঠস্বরটি কর্ণগোচর হতেই চকিতে পিছনে ফিরল, আন্টি! এই আহ্লাদ শব্দ উচ্চারণ করে। অনেক বছর দেখা হয়নি আমাদের, ওরা গুরগাঁওতে থাকে, দিল্লির পাশেই, আর কাণ্ড দ্যাখো, কত দূরের অচেনা আকাশে, ভাসতে ভাসতে দেখা হল। খুব আনন্দে এলুম, সুনাম যথাসাধ্য যত্ন করল আন্টিকে। সে ছোট্ট সুনাম, যার দু বছরের জন্মদিনের পার্টি আমার স্পষ্ট মনে আছে, সে এখন এক বড় কোম্পানির বড় সাহেব। অ্যাপোলো টায়ার্সের ফ্রাংকফুর্ট অফিস থেকে বিজনেস ক্লাসে ডারবানের অফিসে আসছে, তিন দিন বাদে কাজ সেরে দিল্লিতে ফিরবে। আজকের দিনে করপোরেট জেটসেটার সুনামকে কাছে পেয়ে খুব ভাল লাগল। এরাই আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম। কর্মব্যস্ত, সদাচঞ্চল, সুপরিকল্পিত জীবযাত্রা ওদের। দেশ আর বিদেশকে ওরা আর আলাদা করে না। সারা বিশ্বে ওদের কর্মলোক। বৌদেরও অভ্যেস হয়ে গিয়েছে এই ছুটোছুটির রুটিন। অনেক কর্মব্যস্ত বৌকেও দেখা যাচ্ছে ইদানীং যাদের কর্মজীবন এরকমই ঘরের বাইরে দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। দিল্লি বোম্বে বাঙ্গালোরই নয়, আজ সিঙ্গাপুর, কাল হংকং পরশু নিউ ইয়র্ক। কিন্তু তাদের স্বামীদের অভ্যেস হয়েছে কি?