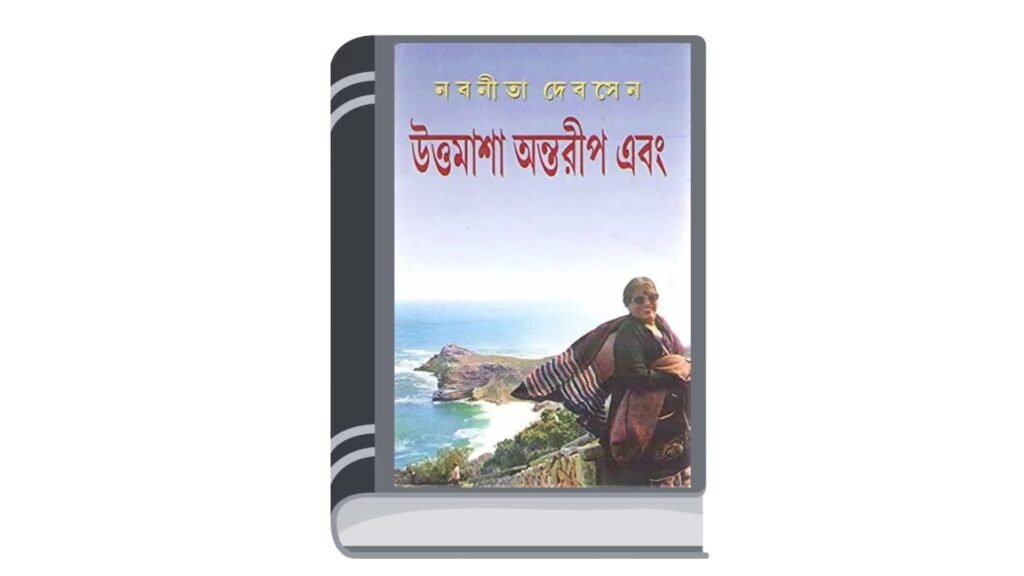ডারবানের পার্বণ, ২১ শে এপ্রিল
২১শে দুপুর বারোটায় ডারবান বিমানবন্দরে আমাকে নিতে এসে অরিন্দমবাবু হাসিমুখে খবর দিলেন, আপনার বান্ধবী তো গতকাল ২০শেই এসে গিয়েছেন কনফারেন্সের জন্যে। আজকে আমার বাড়িতে বাঙালিদের ডিনারে তাতেও নিমন্ত্রণ করেছিলাম আপনাকে মীট করতে, কিন্তু উনি বললেন উনি খুব দুঃখিত, আরেকটা ডিনারে ব্যস্ত আছেন. ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স কনফারেন্সের জন্য কনসাল জেনারেল শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংগ্লে আপনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, আজকেই রেজিস্ট্রেশন করে দেবার জন্য আপনার নামও লিখিয়ে দিয়েছেন। আমরা চাই আপনিও থাকুন। মন্ত্রী রেণুকা চৌধুরী ও তাঁর মেয়ে আসছেন। কাল কনসাল জেনারেলের ডিনারে তাঁদের সঙ্গে আপনার দেখা হবে। গান্ধিজির নাতনি ইলা গান্ধির সঙ্গেও আলাপ হবে। দুটি ডিনারের ফর্মাল আমন্ত্রণপত্র তক্ষুনি আমার হাতে তুলে দিলেন অরিন্দম।
বান্ধবী ২৩শের বদলে আগের নির্দিষ্ট তারিখেই ২০শে এসে গেছেন শুনে আমি কিঞ্চিৎ হতচকিত হলেও প্রকাশ না করে বলি, কিন্তু হায়, আমি যে ঐ মেয়েদের কনফারেন্সে থাকতে পারছি না? আমার টিকিট তো একবার জরিমানা দিয়ে বদল করা হয়ে গিয়েছে, তা ছাড়া কাল রাত্রে যে কেপটাউনের কনসাল মহোদয়ার বাড়িতে প্রফেসর অমর্ত্য সেনের সম্মানে এক ডিনারে আমার আর আমার মেয়ের নেমন্তন্ন আছে? এয়ারপোর্টে আমার মেয়ে আমাকে পিক-আপের ব্যবস্থা করেছে, সব গোলমাল হয়ে যাবে। আমি বরং চলেই যাই। কনফারেন্সের নিমন্ত্রণ তো আগে আমার ছিল না! দয়া করে রেজিস্ট্রেশন ক্যানসেল করে দিন। আমি এখানে তীর্থ করতে এসেছি। মিটিং থাক।
কয়েকদিন পরে যখন শ্রীমতী রুচিরা কাম্বোজের বাড়িতে (কেপটাউনে ভারতের কনসালের পদে আপাতত তিনিই আছেন) মন্ত্রী মহাশয়া শ্রীমতী রেণুকা চৌধুরীর সম্মানে আয়োজিত অন্য একটি ডিনারে রেণুকা ও তাঁর তথ্যচিত্রকার কন্যা পূজার সঙ্গে দেখা হল, এবং ডারবানের সম্মেলনের গল্প শুনলুম, তখন কিন্তু মনে হল, যে অন্তত একদিনের জন্যও কনফারেন্সটিতে যোগ দিলে ভাল হত, সেখানে আমার কিছু শিক্ষার ছিল। আফ্রিকার ও বাইরের মোট পাঁচ হাজার নারীর সমাবেশ হয়েছিল। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে রেণুকা ব্যবস্থাপকদের নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন, সামনের বছরে এই সম্মেলন ভারতে অনুষ্ঠিত হবে। আরো জানলুম, উইনি এসেছিলেন, মঞ্চেও ওঠেননি, বক্তৃতাও দেননি। কিন্তু আফ্রিকান মেয়েরা সবাই ওঁকে সমস্বরে মাম্মা উইনি বলে উচ্চকণ্ঠে সমাদর জানিয়েছিল সভাতে।
মাম্মা উইনি
ঐ একটি সমবেত কণ্ঠের সম্ভাষণেই বোঝা গেল উইনিকে এদেশের কিছু মানুষ এখনও কত ভালবাসে। বিশেষ করে মেয়েরা।
কিন্তু তার উল্টোও আছে। এদেশে ঘুরতে ঘুরতে মানুষের সঙ্গে কথা বলে মনে হচ্ছে অনেকের মনে দুঃখ, উইনি ভুল করেছেন।
স্টম্পি নামে ১৪ বছরের ছেলেটিকে খুনের মামলায় উইনি আইনত নিরপরাধ সাব্যস্ত হয়েছেন বটে, কিন্তু তাতে মানুষের কাছে তাঁর দোষ কাটেনি। হ্যাঁ, খুনি তিনি নিজে নন, কিন্তু তাঁর মদতে পুষ্ট ছিল খুনিরা। উইনিকে অনেকের নৈতিক কারণে দোষী মনে হয়, তিনি শেষ পর্যন্ত আদালতে একবারও দুঃখপ্রকাশ করেননি বলে। আদালতে বারবার ওকে শুধু সেটুকু বলতে অনুরোধ করা হয়েছিল, কেননা যারা মেরেছিল তারা উইনির বাড়িতেই থাকত, ম্যাণ্ডেলা নামাঙ্কিত একটি ফুটবলের দলের সদস্য সকলেই। তারা নির্দ্বিধায়, সর্বসমক্ষে, দিনের আলোয় একে ৪৭ কাঁধে নিয়ে ঘুরত। তা সত্ত্বেও পুলিশ তাদের কিছু বলত না দেখে উইনি তাদের পুলিশের লোক বলে সন্দেই করেননি। উইনি অন্ধ ছিলেন, ওরাই যে আসলে পুলিশের চর সেটা বোঝেননি, পরে বুঝেও ভুল স্বীকার করতে চাননি। অথচ ঐ মৃত ছেলেটি আসলে ছিল উইনির ভক্ত, প্রকৃত বিপ্লবী, যাকে ওরা অমানুষিক অত্যাচার করে স্পাই বলে মেরে চটকে পিণ্ডবৎ করে ফেলেছিল। খুনি বলে যাকে ধরা হল, সে স্বীকার করল খুন করেছে, কিন্তু উইনির আদেশে, উইনিকে জানিয়ে এবং স্টম্পিকে চাবুক স্বয়ং উইনি মেরেছিলেন। সারা দেশ কেঁদে উঠেছিল। উইনির সেই ব্যাখ্যাতীত নিষ্ঠুর আচরণে উইনির ভক্তরা অনেকেই তাঁকে সাময়িকভাবে উন্মাদগ্রস্ত বলে মনে করেছেন। কালক্রমে উইনির অনেক বদভ্যাস হয়েছে, প্রচণ্ড পানাশক্তি, প্রচণ্ড মাদকাশক্তি, আর নিত্য নবীন তরুণতর প্রেমিকে অনির্বাণ আসক্তি, এই সব উদ্দামতা তাঁকে সুস্থ মস্তিষ্কে সিদ্ধান্ত নেবার উপযুক্ত থাকতে দেয়নি, বলেছিলেন, পিপা আর ম্যালকম স্টাইন। দক্ষিণ আফ্রিকার পুরনো ইহুদি পরিবারের বামপন্থী মাঝবয়সী অধ্যাপক দম্পতি। অত্যন্ত চমৎকার মানুষ, ম্যালকম উইটসে ড্রামার প্রফেসর ছিলেন, এখন জোবর্গের বিখ্যাত মার্কেট থিয়েটারের আর্টিস্টিক ডিরেক্টর। ফিলিপা (ডাক নাম পিপা) এখনও উইটসে পড়াচ্ছেন, সাক্ষরতা, প্রাথমিক শিক্ষা আর স্বাস্থ্য নিয়ে তাঁর বর্তমান কাজ। জোবর্গে এঁদের সঙ্গে এতই ভাব হয়ে গেল যে পরের সপ্তাহে কেপটাউনে চারদিনের ছুটি কাটাতে এসে ওঁরা আমাদের নিয়ে সাউথ আফ্রিকার সঙ্গে পরিচয় করাতে লাগলেন। এক সন্ধ্যায় দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান, এবং পৃথিবীর জীবিত নাট্যকারদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার আঠোল ফুগার্ডের নবতম নাটকটি দেখালেন, কেপটাউনের প্রসিদ্ধ থিয়েটার ব্যাক্সটার থিয়েটারে। একই বাড়ির মধ্যে সিনেপ্লেক্সের মতো থিয়েটাপ্লেক্স, তিনটি তিন রকমের প্রেক্ষাগৃহ ও নাট্যমঞ্চ আছে। আমরা সবচেয়ে ওপরের তলায় একটি ছোট্ট গোল প্রেক্ষাগৃহে ভিক্ট্টি নাটকটি দেখলুম। সাদা কালোর দ্বন্দ্ব নিয়েই কাহিনি, উত্তেজনা টান টান, ডায়লগ স্মার্ট, অভিনয়ের মানও যথেষ্ট উঁচু। তবুও নাটকটি আমার মন ভরাতে পারেনি। দুর্বলতা আসলে নাটকেই। ঠিক জমাতে পারেননি নিজের বক্তব্যটি। অনেকদিনই ফুগার্ড ক্যালিফোর্নিয়ার বাসিন্দা সেখান থেকেই দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিয়ে নাটক লিখে চলেছেন।
ওরা একদিন আমাদের ইতালীয় ডিনার খাওয়ালেন এবং একদিন দুজনে মিলে আমাদের নিয়ে সারা সকালভোর অতলান্তিকের এবং ভারত মহাসাগরের বিভিন্ন সমুদ্রসৈকতে ঘুরে বেড়ালেন ঝিরিঝিরি বৃষ্টির মধ্যে। কেপটাউনের হেমন্ত আর শীতকালের এই চিরাচরিত বৃষ্টি, এটা এপ্রিল মাস, এখানে এখন শীত নামছে, হেমন্তকাল। সেই বৃষ্টিভেজা সকালে, দুপুর বলাই ঠিক, সমুদ্রতীরের এক রেস্তোরাঁতে একসঙ্গে ব্রাঞ্চ খেতে খেতে আবিষ্কার করলুম যে আমার প্রিয় ছাত্রী রিমলি এখন পিপার খুব বন্ধু, ওরা দুজনে এবং আরেকজন মেয়ে, তিন মহাদেশে স্কুলের শিক্ষা নিয়ে একটি প্রজেক্টে যুক্ত। কোথা থেকে কার সঙ্গে কোন সুতোর গেরোতে কে যে বাঁধা পড়ে। এদের সঙ্গেই উইনি বিষয়ক আলোচনা হচ্ছিল। উইনি বিষয়ে সাধারণ মানুষের মনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া।
সোয়েটোতে বেড়ানোর সময়ে উইনি ম্যাণ্ডেলার বাড়ি, দেখাতে দেখাতে সোফিসা যা বলেছিল। কেপটাউনে আমাদের কার্লাড ড্রাইভার অব্রের মনোভাব তার বিপরীত। সে মেয়ে তো আদৌ ভাল নয়, ১৪ বছরের বাচ্চা ছেলেটাকে খুন করিয়েও নিজে দিব্বি মুক্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার টাককড়ি কিছুরই অভাব নেই। অনেক অন্যায় করেছে উইনি। ম্যাণ্ডেলা কি আর অমনি অমনি ওকে ছেড়েছেন?
—অরে একাই শুধুই এককরম মনে করে তা নয়। অনেকেরই মনের ভাব এরকম। আকর্ষণীয়া, সুন্দরী, চটকদার, স্বভাব-প্রণয়ী, বুদ্ধিমতী এবং খ্যাতির আলোতে ঝলমলে উইনির ষাট বছর বয়সেও প্রচুর বিশ -এর তরুণ প্রণয়ী ছিল, ঐ কুখ্যাত ফুটবলের দলেও ছিল তারা বেশ কয়েকজন। স্টম্পির মৃত্যুতে তাঁর এমনই এক প্রণয়ীর হাত ছিল বলে শোনা যায়। ১৯৯০তে নেলসন ম্যাণ্ডেলা যখন কারগার থেকে মুক্ত হলেন, তখন উইনির প্রবল প্রেম চলছে ডালি নামে আর এক যুবকের সঙ্গে। উইনি স্বামী ম্যাণ্ডেলাকে স্পষ্ট বললেন, তিনি ডালিকে পরিত্যাগ করতে পারবেন না। তক্ষুনি ম্যাণ্ডেলা কিছু বলেননি। মুক্তি পাবার পরে ম্যাণ্ডেলা দম্পতি যখন বিদেশ ভ্রমণে বেরুলেন, উইনি ডালিকেও সঙ্গে নিলেন। সর্বত্র ডালির ঘর থাকত পাশেই। সারাদিন স্বামীর সঙ্গে জনসংযোগে ব্যাপৃত থাকলেও উইনি নিশিযাপন করতেন ডালির ঘরেই। নেলসনের ঘরে নয়। নেলসনের পক্ষে এতটা সহ্য করা কঠিন হল। ফিরে এসে কিছুদিনের মধ্যেই ম্যাণ্ডেলা প্রেস কনফারেন্স ডেকে জানালেন তিনি আর উইনি বিচ্ছেদের কথা ভেবেছেন। এবং সেই প্রেস কনফারেন্সের ঘর থেকে কোনও মানুষই নাকি শুকনো চোখে বাইরে আসেননি, সাংবাদিকরাও না, ম্যাণ্ডেলা নিজেও না। বজ্রপাতের মতো এসেছিল খবরটা দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষদের মধ্যে, কেউ এটা ভাবেনি, যদিও উইনির পুরুষ-সঙ্গের কথা উইনি গোপন করতেন না। এই গল্প শুনেছিলুম পিপার মুখে। তিনিও মনে হল, উইনির রীতিমতো ভক্ত। বিদারিত হৃদয়ে পিপা বলেছিলেন, ভাবতে পারো বোকা মেয়েটি অবিশ্বাসী প্রেমিকের জন্য কী ছেড়ে দিল? এতদিনের চেষ্টায় গড়ে তোলা বিপ্লবী নায়িকার ইমেজ, স্বাধীন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্টের স্ত্রী, ফার্স্ট লেডি হবার সম্মান ও ক্ষমতা! সারা সাউথ আফ্রিকা ওকে মাম্মা ম্যাণ্ডেলা বলত। মাম্মা উইনি বলত। সেই সিংহাসনটা অকারণে ছেড়ে দিল। কীসের জন্যে? কার জন্যে প্রেম? ভোগলালসা? কী বা সেই ভোগ? স্বাধীনতার জন্যে উইনির এতদিনের পরিশ্রমের ফসল তোলবার সময় এসেছিল এখনই। সমগ্র বিশ্বের সম্মান পাবার সময় এসেছিল। সব নষ্ট করে নয়ছয় করে ফেলল। হ্যাঁ নতুন স্ত্রী গ্রাস খুব চমৎকার মেয়ে, বুদ্ধিমতী, অভিজাত, গ্রেসফুল, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীনতার ইতিহাসের ঐ জায়গাটাতে সে কোনওদিনই যেতে পারবে না। তার আজন্মের বেড়ে ওঠাই আলাদা। কিন্তু মানুষটা ভাল।
–সেই প্রেমিক নিশ্চয়ই আর নেই উইনির জীবনে?
–ডালি? না না, অনেকদিনই নেই। ডালি এখন এস এ বি সি-র প্রধান, সাউথ আফ্রিকান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন। বিশাল ব্যাপার। তার কোনও ক্ষতি করেনি কেউ। তরুণী উইনিরও তিয়াত্তর হল। এখনও খুব সুন্দরী। চিরতরুণ নেলসন কিন্তু এতদিন সত্যিই বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন।—পিপা বলে, ‘সেদিন আমরা প্রফেসর অমর্ত্য সেনকে নিয়ে গিয়েছিলাম ওঁর সঙ্গে দেখা করতে। কবে এলে? কোথা থেকে এলে? এখান থেকে কোথায় কোথায় যাবে? দক্ষিণ আফ্রিকা কেমন দেখছ? এই সব বলছিলেন কোনও গভীর অলোচনার ক্ষমতা নেই আর। কোনও বিষয় ধরে রাখতে পারেন না ঠিক। গ্রাসই প্রধানত কথাবার্তা চালাচ্ছিল। এইচ আইভি এইড্স আর শিশুদের শিক্ষা স্বাস্থ্য এই সব নিয়ে ওর কাজ। মেয়েটি সুবুদ্ধিমতী।’
—ওর বয়স কত? ম্যাণ্ডেলার তো আশি পেরিয়ে গিয়েছে।
—গ্রাসের? এই পঞ্চাশ পঞ্চান্ন হবে। ভাল কাজকর্ম করছে।
ম্যাণ্ডেলার বর্তমান স্ত্রী গ্রাস (গ্রেস) একদা মোজাম্বিকের প্রেসিডেন্টের স্ত্রী ছিলেন, সেই যিনি প্লেন ক্র্যাশে মারা যান দক্ষিণ আফ্রিকার আকাশেই। খুব প্রগতিবাদী মানুষ ছিলেন। মোজাম্বিকের জন্য, কালো আফ্রিকার জন্য তাঁর চোখে আধুনিকতার স্বপ্ন ছিল। মনে করা হয় তাঁর মৃত্যু স্বাভাবিক দুর্ঘটনা নয়। আপারথেইডবাদী দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারি চক্রান্তের শিকার তিনি। তাঁর প্লেনকে ইচ্ছে করে ভুল সিগনাল দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সন্দেহ সন্দেহই থেকে গিয়েছে, কিছুই সেভাবে প্রমাণিত হয়নি। তাঁরই বিধবাকে নেলসন ম্যাণ্ডেলা বিবাহ করেছেন উইনির পরে।
সৌভাগ্যক্রমে আমাদের জ্ঞানপীঠের সভামঞ্চে ম্যাণ্ডেলা ও তাঁর নব বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে দিল্লিতে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল, ম্যাণ্ডেলা মহাশ্বেতা দেবীকে পুরস্কার দিতে এসেছিলেন যখন। দুজনকেই সজীব, বুদ্ধিমান এবং গ্ল্যামারাস মনে হয়েছিল আমার। সুন্দর বলেছিলেন ম্যাণ্ডেলা। মহিলা সুন্দরী, হাস্যমুখী কিন্তু লাজুক। তখন অন্তত আলাপী ছিলেন না।
উইনি পুনর্বিবাহ করেননি। উইনির বহুগামিতা জনগণের মার্জনা পেয়েছিল, কিন্তু কিশোর স্টম্পির খুনটা ক্ষমা পায়নি। তা সত্ত্বেও জোহানেসবর্গে, ডারবানে, কেপটাউনে বিভিন্ন স্তরের বেশ কিছু মানুষের অনুভূতিতে দেখলুম উইনি এখনও মাম্মা উইনি। সবকিছুর পরেও।
বাসনা যখন বিপুল ধুলোয় অন্ধ করিয়া অবোধে ভুলায় • এইচ আই ভি আর এইড্স
পিপা বলেছিলেন আফ্রিকাতে যৌনজীবনের ধারণা আমাদের চেয়ে একেবারে অন্যরকম, আমাদের পক্ষে বোঝাও কঠিন। বহুচারিতাতে দোষ ধরে না কেউ। না পুরুষের না নারীর এটাই দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বনাশের কারণ, এইচ. আই ভি-র প্রসারে। পৃথিবীতে সর্বোচ্চ সংখ্যার এইচ আই ভি রোগী আছে এখন দক্ষিণ আফ্রিকাতে।
কথাপ্রসঙ্গে পিপা তাঁর এক ছাত্রীর গল্প করলেন। পিপা তাকে জিজ্ঞেস করেছেন, তোমার কটা বয়ফ্রেণ্ড এখন? সে বলেছে একজন ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টার, একজন এন্টারটেইনমেণ্ট মিনিস্টার, একজন টেক্সটাইল মিনিস্টার, একজন ফুড মিনিস্টার, একজন এডুকেশন মিনিস্টার আর একজন হোম মিনিস্টার।
—তার মানে? এতগুলি মিনিস্টার তোমার বয়ফ্রেন্ড? কী কাণ্ড? তাদের বয়েস কত?
সে হেসে খিলখিল করে বলল,—মানে একজন ফ্যান্সি গাড়ি যোগায়, একজন সিনেমা থিয়েটারে নিয়ে যায়, একজন পোশাক-আশাক কিনে দেয়, একজন রেস্তোরাঁতে খাওয়ায়, একজন ইউনিভার্সিটিতে পড়ার খরচা জোগায় আর একজনের বাড়িতে থাকি। মোট ছ জন বয়ফ্রেণ্ড। এতে তার লজ্জা নেই, রীতিমতো গর্বের বিষয়। একইসঙ্গে একধিক যৌনসঙ্গী থাকার ফলেই এ দেশে এরকম প্রচণ্ড গতিতে এইচ আই ভি আর এইড্স ছড়াচ্ছে। ১৫থেকে ২৫এর মেয়েদের মধ্যে সবথেকে বেশি। গ্রামাঞ্চলে শহরের চেয়ে বেশি কেননা সেখানে কেউই কোনও সাবধানতা নেয় না। মেয়েরা বরং জড়ি বুটি উদ্ভিদ ইত্যাদি ব্যবহার করে যোনির অভ্যন্তরটি শুকনো করে রাখে যাতে পুরুষেরা সেই শুকনো যোনিপথে প্রবেশের রুক্ষ সুখ পায়। এটা দক্ষিণ আফ্রিকার কালো পুরুষমানুষদের মন-পসন্দ, সিক্ত নয়, শুষ্ক যোনিপথ ঘর্ষণে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় নারীর গোপন অভ্যন্তর। মহান পুরুষজাতি প্রেমের পথে কোনও বাইরের বাধাবিঘ্ন কণ্ডোম ইত্যাদি এক্কেবারে পছন্দ করেন না। এবং যোনিপথের ক্ষতস্থানের ফলে এইড্স এইচ আই ভি ছড়িয়ে পড়াও সহজ হয়। শুনলুম এখানকার গ্রামীণ নিয়মে ১২ বছরের ছেলেরা আলাদা একটি নিজস্ব ঘর পায়, যেখানে সে নারীসঙ্গ করতে পারে। মেয়েরা ১৪ হতে না হতে মা হয়ে পড়ে। দক্ষিণ আফ্রিকার ভয়াবহ যৌন জীবনের প্রায় এই একই কাহিনি সর্বত্র শুনেছি। একবার শুনেছি ডারবানে, একবার জোবর্গে, আর একবার কেপটাউনে, বিভিন্ন ধরনের মানুষের মুখে।
ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রী পিপা এখন সাক্ষরতা, প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করছেন। বললেন, বর্তমান প্রেসিডেন্ট এম্বেকি নানাভাবে প্রগতিবাদী নেতৃত্ব দিচ্ছেন দেশকে। মেয়েদের অনেকখানি সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষমতা এনে দিয়েছেন, পার্লামেন্টে এখন প্রচুর মেয়ে। সবাই খুব বাকপটু। নানা দায়িত্বপূর্ণ সরকারি উচ্চপদে মেয়েদের নিয়োগ করেছেন। ম্যাণ্ডেলার চেয়েও ইনিই বেশি করে নারীদের নিয়ে ভেবেছেন, উন্নয়নের নানা প্রকল্পও নিয়েছেন। সবই তো ভাল শুধু এইচ আই ভি-র বেলাতে তাঁর অবিশ্বাস্য সব সরল এবং ক্ষতিকর নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক মন্তব্য আছে। এইসের সঙ্গে নাকি এইচ আই ভি-র কোনও যোগই নেই। এইড্স হয় দারিদ্র্য থেকে, পুষ্টির অভাবে, ভাল খেলেদেলেই আর এইড্স হবে না। (অর্থাৎ ধনী হলেই এইড্রসের ভয় তাহলে নেই?) প্রেসিডেন্ট স্বয়ং এবং তাঁর সঙ্গী ভাইসপ্রেসিডেন্ট জুমা (তিনি আবার নারীধর্ষণ-এর অভিযোগে কাঠগড়াতে চড়েছেন) এই দুজনে মিলে এইড্স বিষয়ে দুর্ভাগ্যজনক যত এলেবেলে আশ্বাসবাণী বারংবার মিডিয়াতে প্রচার করার কুফলে সাধারণের বিপুল বিভ্রান্তি ঘটেছে, এবং এইডস অনেকখানি ছড়িয়ে পড়েছে এদেশে। এতদিনে প্রেসিডেন্ট এম্বোকি দিব্যজ্ঞান লাভ করে অনুশোচনা বোধ করেছেন, সম্প্রতি অন্য সুরে কথা বলতে শুরু করেছেন, এবং সারা দেশে সচেতনতা সৃষ্টির কাজ জোরকদমে চলেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অচিরেই এদেশে এইচ আই ভি আর এইড্স মহামারীর করাল রূপ ধারণ করবে। সারা পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র আমাদের ভারতবর্ষেরই এক নিদারুণ প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে দেবার সম্ভাবনা রয়েছে ২০১০-এর পরে। অবশ্য মহাচীন তো কিছুই জানায় না। কে জানে সেখানে মহাপ্রাচীরের অন্তরালে কী ঘটেছে?
ডারবানে এসে অরিন্দমের মুখে এই এইড্স ভীতির প্রসঙ্গ, এই টিনএজারদের চট করে হাতে নগদ টাকা পাওয়া ও ভাল ভাল পোশাক কেনার লোভে যথেচ্ছ যৌন বেচালের কথা, অবাধ-অবোধ, অনাচারের কারণে অকালে কালরোগ ও মৃত্যু, যার প্রতিফলে দশ বছরের মধ্যে এদেশে আর তরুণ-তরুণী থাকবে না, ইত্যাদি ভয়াবহ কথা শুনেছি। জোহানেসবর্গে অবিকল একই কথা শুনে এসেছি, এবং কেপটাউনে গিয়েও পিপা ম্যালকমদের মুখে এবং পার্লামেন্ট নাটাল অঞ্চলের প্রতিনিধি এম পি মেওয়া রামগোবিনের মুখেও এই একই প্রসঙ্গ শুনলুম। এইডস ও আফ্রিকার সংকটাপন্ন ভবিষ্যৎ নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার সকল শিক্ষিত চিন্তাশীল মানুষই উদ্বিগ্ন। যেন প্রলয়ের মুখোমুখি। কিন্তু ভারতেও তো এইচ-আই ভি-র সংকট কিছু কম নয়। বরং কুসংস্কারের ফলে চিকিৎসা ও শুশ্রূষার অভাবে রোগীদের সংকট অনেকগুণ বেশি। কিন্তু পথেঘাটে এত আলোচনা তো শুনি না? যথেষ্ট উদ্বিগ্ন তো নই আমরা? প্রবলভাবে এইড্স কন্ট্রোলের চেষ্টা কই সরকারের? কোথায় শুশ্রূষা? কোথায় চিকিৎসা? খবরে পড়ি সরকারি হাসপাতালেও এইড্স রোগী ফিরিয়ে দিচ্ছে অদ্যাবধি। ডাক্তার নার্সেরাও রোগী স্পর্শ করতে ভীত। তাঁদের জ্ঞানের পরিধি লজ্জাজনকভাবে সংকীর্ণ এবং স্পষ্টতই শিক্ষা অসম্পূৰ্ণ। সরকারকে আরো করিৎকর্মা হতে হবে, শুধু এন জি ও-গুলি কত করবে? যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সরকারি ও বেসরকারি দ্বৈত উদ্যোগ ছাড়া আত্মরক্ষা সম্ভব নয় আমাদের, সহৃদয় সচেতনতা ছাড়া কাটানো যাবে না ভারতবর্ষের এই দুরূহ সংকট। আফ্রিকার কালো মেয়েরা বড় লাবণ্যময়ী, সুন্দরী এবং সেক্সি। আপাতত এদের অধিকাংশের ভবিষ্যত এত স্বল্পায়ু ভেবে আমার খুব মন খারাপ হয়ে গেল। দারিদ্র্যের জন্য অনন্যোপায় হয়ে দেহ-বিক্রি এক জিনিস। আমাদের দেশে জি টি রোডের ধারে ধারে গ্রামগুলিতে মেয়ে বৌদের মধ্যে যেভাবে ছড়িয়ে পড়ছে এই মারণ রোগ, ট্রাকড্রাইভারদের মাধ্যমে, তাদের কথাও মনে হল। কিন্তু বিলাসে ব্যসনে ভোগের জন্য ব্যয় করবার লোভে অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহের কারণে প্রাণসংশয় করে মধ্যবিত্ত মেয়েদের এই দেহোপজীবিনী বৃত্তি গ্রহণের মধ্যে শুধুই বেদনা আছে।
এ মানসিকতা আমাদেরও অচেনা নেই আর। ভারতবর্ষেও শহরে শহরে ঝলমলে মল-গুলির নেশা চটজলদি উপার্জনের লোভে এক ধরনের উচ্চাশী ছাত্রীদের এবং তরুণী গৃহবধূদের কলগার্লের পেশায় মাতিয়ে তুলছে। তাদের অর্থনৈতিকতার দিকটা নিয়েই আমাদের যত সতী সাবিত্রীর ধর্মাধর্মের চিন্তা, যত উদ্বেগ। কিন্তু আরো বড় সর্বনাশ, দুরারোগ্য করাল ব্যাধির দিকটা নিয়ে আমরা এখন সেভাবে ভাবছি কি? সর্বদা কি ওরা সতর্কতা অবলম্বন করে? থ্যাইল্যাণ্ড ও বার্মার গ্রামগুলির মতো এবারে এদেশেরও পরিবারের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে বিষ রোগ।
দক্ষিণ আফ্রিকাতে কিন্তু রাস্তাঘাটে এই বিষয়ে সাধারণকে কোনও ধরনের জরুরি জ্ঞান বিতরণের হোর্ডিংয়ের উদাহরণ চোখে পড়ল না। অবশ্য হতেই পারে, হয়তো আমার চোখ এড়িয়ে গিয়েছে, কেননা আমি ঐ তিন সপ্তাহ কোনও খবরের কাগজ পড়িনি, কোনও টিভি দেখিনি, শুধু মানুষ দেখেছি।
তীর্থভ্রমণ
ডারবানে নেমে প্রথমে গেলুম কনসাল জেনারেল শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার বাড়িতে, সেখানেই আমার রাত্রিবাসের ব্যবস্থা। লাঞ্চ খেলুম শ্রীমতী হেমল শ্রিংলার সঙ্গে, তিনি তরুণ কনসাল জেনারেলের সুন্দরী তরুণী স্ত্রী। কম্পারেটিভ লিটারেচারে পি এইচ ডি করছেন সিটি ইউনির্ভাসিটি অফ নিউ ইয়র্ক থেকে। বিষয় ইংরিজিতে লেখা ভারতীয় নভেল। আমাকে দেখে খুব খুশি, এক লেখিকার আসার কথা জেনেছিলেন, কিন্তু আমি যে তুলনামূলক সাহিত্যের মাস্টারমশাই হই, সেটা জানতেন না। মীনাক্ষী মুখার্জি, বইগুলির কথা এখনও জানেন না দেখে অবাক হয়ে রেফারেন্সগুলি দিলুম, ভারতীয় ইংরিজি নভেলের ওপরে তাঁরই প্রথম জরুরি কাজ।
এই পরিবারটিকে অসামান্য মনে হল, হর্ষবর্ধন শ্রিংলে দার্জিলিং-এর লোক, তাঁর স্ত্রী বম্বের গুজরাতি মেয়ে। তাদের এক আট বছরের পুত্র আছে। আপাতত হর্ষের বাবা-মা এসেছেন। হেমল শ্বশুরবাড়ির নানা অতিথি সামলে তার ওপরে শংকরাকে ডাকার মতোই আমাকে ডেকে এনেছেন। যারপরনাই আন্তরিক যত্ন আত্তিও করছেন। তাঁর শ্বশুর -শাশুড়িও চমৎকার মানুষ আমাকে পরিবারের একজনের মতো আদর আপ্যায়ন করলেন। অনেক বছর আগে আমি যখন স্পেনে গিয়েছিলুম, সেখানেও একজন দার্জিলিং-এর বাসিন্দা অ্যাম্বাসাডর ছিলেন, চমৎকার মানুষ। আমাকে অন্যত্র থেকে তুলে এনে জোর করে বাড়িতে রেখেছিলেন। এঁরা তাঁকে চেনেন। মিস্টার আটুক। শ্রিংলা সিনিয়র বললেন, আটুক অল্পদিন আগেই মারা গিয়েছেন। শুনে মন খারাপ হল, আটুক আমাকে মোটে চিনতেন না, একা ভারতীয় মহিলা এসে ইতিউতি ঘুরছেন শুনেই বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। শ্রিংলা দম্পতি মস্ত বড় একটি ঘর ও স্নানঘর দিয়েছেন আমাকে বাগানের লাগোয়া। সবুজ ছায়া ভরা, পুরনো কাণ্ড আর ঝুরিওয়ালা একটি অচেনা বৃক্ষ ঠিক আমার জানালার সামনে। চেনা নয়, অথচ দেখলেই কার জন্যে যেন মন কেমন করে ওঠে।
ফিনিক্স সেটলমেন্ট
লাঞ্চ খেয়েই অরিন্দম আর তার দিল্লিতে পড়ুয়া পুত্র অনির্বাণের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি ফিনিক্স সেটেলমেন্টের উদ্দেশ্যে। এই নাটাল প্রদেশে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক ভারতীয়ের বসবাস। হিন্দু, মুসলমান পার্সি, ক্রিশ্চান সব ধর্মের ভারতীয় মানুষই এসেছিলেন তাদের সবারই পরিচয় ছিল কুলি। ১৮৯০থেকে এখানে আখের খেতে চাষের কাজ করাতে তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, বিহার থেকে ক্রীতদাস নিয়ে আসা হত পাঁচ বছরের কড়ারে। তার পরে তাদের ইচ্ছে করলে তারা আবার দু বছর করে চুক্তিবদ্ধ হতে পারতো, কিন্তু জমি বাড়ির অধিকারী হতে পারতো না? চুক্তিপত্র থেকে মুক্তির পরেও। থাকতে চাইলে সেই বসবাসের অধিকারের জন্য সরকারকে তাদের বার্ষিক শুল্ক দিতে হত এবং তাদের পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচনের ভোটাধিকার দেওয়া হত না।
স্বাধীনতার পরে আইনকানুন বদল হয়েছে, আজ আর তাদের পরিবারের সদস্যরা কেউ ক্রীতদাস নন, সবাই প্রতিষ্ঠিত, স্বাধীন নাগরিক। কেউ ব্যবসা করেন, কেউ চাকরি। আট লক্ষ ভারতীয় আছেন নাটালে, তাদের মধ্যে ৬ লক্ষ নাকি একদা ছিলেন তামিল আর তেলুগুভাষী, সে ভাষা অবশ্য তাদের বর্তমান প্রজন্মের নব্বুই ভাগের আর আয়ত্তে নেই। বাকিদের মধ্যে ৭০ হাজার গুজরাটি ব্যবসায়ী, অধিকাংশ মুসলমান। প্রথমে অনেক আগে কিছু ভারতীয় মুসলমান বণিক এয়েছিলেন মরিশাস থেকে, তারা নিজেদের আরব বণিক বলতেন। তারপরে পশ্চিম ভারত থেকে গুজরাটি মুসলিম বণিকরা নিজেরাই ভাগ্যসন্ধানে এসেছেন, ব্যবসার উদ্দেশ্যে। মুচলেকা দিয়ে দাসত্ব করতে নয়। ভারতীয় মুসলমানরাও ইংরেজি পোশাক না পরে মধ্যপ্রাচ্যের পোশাক পরতেন এবং নিজেদের আরব বলে পরিচয় দিতেন, চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের থেকে নিজেদের আলাদা রাখবার উদ্দেশ্যে। তাঁরা অবস্থাপন্ন ছিলেন। তবু তাদের কুলি নাম ঘোচেনি।
এমনই একজনের হয়ে মামলা লড়তে লন্ডনের এক তরুণ ভারতীয় ব্যারিস্টার একদা এসেছিলেন নাটালে। তার পরের ঘটনা ইতিহাস। গান্ধিকে এনেছিলেন আবদুল্লা শেঠ, সম্ভ্রান্ত গুজরাটি ব্যবসায়ী, ধনী ও সৎ। বাদামিরা সবাই তো কুলি, ভারতীয় বণিক কুলি বণিক, গান্ধির ও পরিচয় ছিল কুলি ব্যারিস্টার। কেপটাউনে ‘নন্দনার সহ অভিনেতা পরভীন একদিন মহা উত্তেজিত হয়ে এসে আমাকে বলল শেঠ আবদুল্লার বংশধরের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে, সেই যিনি গান্ধিজিকে এদেশে এনেছিলেন। ইনি দক্ষিণ আফ্রিকার বিখ্যাত এক নবীন ফিল্ম প্রোডিউসার, সপরিবারে এখনও ডারবাইনে থাকেন। নাম এ বি মুসা। ঠিক কি ভুল জানি না কিন্তু এ তো হতেই পারে। আমাদের অজানিতে পায়ে পায়ে জড়িয়ে ধরে ইতিহাস।
হিন্দি ঔপন্যাসিক শ্রীগিরিরাজ কিশোর দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছিলেন গান্ধিজিকে নিয়ে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের নিয়ে একটি উপন্যাস লিখবেন বলে। অসামান্য উপন্যাস লিখেছেন, সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারও পেয়েছিলেন সেই বই-এর জন্যে, পহেলা গিরমিটিয়া, মানে এগ্রিমেন্ট। বিহারী কুলিরা এগ্রিমেন্ট উচ্চারণ করতে পারতো না বলে নিজস্ব শব্দ তৈরি করে নিয়েছিল। সেই শব্দ এমনভাবে চালু হয়ে গিয়েছিল, যে চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিকদের দলিলেও এগ্রিমেন্ট অর্থে এই গিরমিটিয়া শব্দটি লিখিত থাকত নাকি। চুক্তিবদ্ধ মজুরদের রক্তে তৈরি ঘোরতর এক শব্দ। যার শৃঙ্খল থেকে সহজে মুক্তি নেই। গাড়ি চলতেই মহম্মদ রফি! আরে? অরিন্দম বললেন, “রেডিওতে হচ্ছে। এখানে দুটো ভারতীয় স্টেশন আছে, লোটাস, আর হিন্দবাণী, সেখানে হিন্দি আর তামিল গান হয়। খুব পপুলার চ্যানেল।”
প্রথমে আমরা গেলুম ফিনিক্স সেটেলমেন্ট। একবার জোহানেসবর্গ থেকে ডারবান যাবার পথে তাঁর এক বন্ধু গান্ধিকে রাস্কিনের আনটু দিস লাস্ট বইটি ট্রেনে পড়তে দিয়েছিলেন। ১৮৬২-তে প্রকাশিত সেই বইতে গান্ধি যেন নিজের মনের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পেলেন। নিজের বিশ্বাস, মূল্যবোধের স্পষ্ট প্রতিফলন দেখলেন অতদিন আগের রাস্কিনের ভাষাতে। (১) ব্যক্তির কল্যাণ সমষ্টির কল্যাণের মধ্যেই নিহিত,(২) একজন আইনজীবী আর একজন পারমাণবিক কাজের সামাজিক সম্মান অভিন্ন, কেননা তারা দুজনেই নিজেদের পেশার শ্রমের মূল্যে জীবনধারণ করে। এই দুটি ধারণা গান্ধির নিজেরও ছিল। তৃতীয়টি নতুন।(৩) পরিশ্রমে যাপিত জীবনের মূল্য বিলাসে যাপিত জীবনের চেয়ে অনেক বেশি, যে হাতে-কলমে কাজকর্ম করে, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরি করে, চাষী, তাঁতি, কামার, কুমোর, ছুতোর, মুচি, তাদের জীবনই ধন্য। তারা মানুষের সেবায় লাগে।
রাস্কিনের ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গান্ধিজির মনের বল অনেক বেড়ে গেল। তাঁর বই পড়বার দশদিনের মধ্যে ডারবান থেকে১৪/১৫ মাইল দূরে, ফিনিক্স স্টেশনের কাছাকাছি গান্ধি অনেকখানি ফাঁকা জমি কিনে ফেললেন, এক হাজার পাউণ্ড দিয়ে, ১৯০৩/০৪ নাগাদ ঝোপজঙ্গল ভর্তি, কিন্তু প্রচুর ফলের গাছ ছিল তারই মধ্যে, গান্ধির সেটাই ভাল লাগল, অজস্র ফলন্ত আমগাছ, কমলালেবুর বন। সেখানে সপরিবারে, সদলবলে, যাঁরা ওর সঙ্গে গুজরাট থেকে গিয়েছিলেন জাহাজে করে তাঁদের ও কিছু ইউরোপীয় সহকর্মী বন্ধুদের নিয়ে ফিনিক্স ফার্ম নামে আদর্শ খামার গড়লেন তিনি। প্রত্যেককে কাজ করবার দায়িত্বে জমি ভাগ করে দেওয়া হল কিন্তু বেড়া দেওয়া হল না। ঠিক হল ডারবান নয় এখান থেকেই বেরুবে তাঁর নতুন সাপ্তাহিক পত্রিকা, ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ান, খরচ বাঁচাতে প্রেস এখানেই সরিয়ে আনা হবে। খামারের কাজের ফাঁকে ফাঁকে নিজেরাই পত্রিকার ও প্রেসের কাজ চালাবেন। ডারবান থেকে ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট প্রিন্টিং প্রেস তুলে আনা হল ফিনিক্সে। সেই প্রথম গান্ধি ভেবেছিলেন সর্বোদয় আশ্রম তৈরির কথা। জোহানেসবর্গের ভারতীয় সব থিয়সফিস্ট বন্ধুদের সংসর্গে এসে তিনি নিয়মিত গীতাপাঠ করতেন। গীতা থেকে অপরিগ্রহ এবং সমভাব জীবনযাপন নিয়ে এই দুটি মূল শিক্ষা তিনি অন্তরে গ্রহণ করেছিলেন, এবং জীবনে পালন করার চেষ্টা করতেন। তার সঙ্গে সোনায় সোহাগা হয়ে জুটল রাস্কিনের ভাবনা। সরল নিরাভরণ জীবন-যাপন, সবাই সমানভাবে গায়ে গতরে পরিশ্রম করবেন, সবাই সমান পারিশ্রমিক পাবেন, মাসিক তিন পাউণ্ড, সকলের কাজের মূল্য সমান সমান, কোনও কাজ অন্য কোনও কাজের চেয়ে বেশি মূল্যবান নয়। জঙ্গল পরিষ্কারের কাজ, বাগান তৈরির কাজ, পত্রিকা প্রকাশনার কাজ, ঘরবাড়ি তৈরির কাজ, সবই করা হবে নিজের হাতে। সগৌরবে তো আশ্রমের কাজ শুরু হল, কিন্তু ঘরদুয়ার নেই, ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে তাঁবু খাটিয়ে বাস, আর চতুর্দিকে সাপের দৌরাত্ম্য। কিন্তু জেদের জয় হল, মাস দুয়েকের মধ্যে নিজেদের হাতে হাতে টিনের চালের কুঁড়েঘর তৈরি হয়ে গেল আটখানা, প্রেসের কাজ শেখা চলল চাষের কাজের সঙ্গে সঙ্গে, আর ১৯০৪ এর ডিসেম্বর যথাকালে বেরিয়ে পড়ল ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ান। প্রথমদিকে এই পত্রিকা চারটি ভাষাতে ইংরেজি, গুজরাটি, তামিল ও হিন্দিতে প্রকাশিত হয়েছিল। শেষকালে অবশ্য হিন্দি আর তামিল বাদ দিতে হয় নানা অসুবিধার কারণে, কিন্তু গুজরাটি ও ইংরেজিতে পত্রিকাটি বেরুতে লাগল নিয়মিত। একগুচ্ছ ভারতীয় এবং ইউরোপীয় আদর্শবাদী মানুষের স্বপ্নচারণের একান্ত আশ্রয় ছিল এই ফিনিক্স সেটেলমেন্টের নতুন উপনিবেশ। গান্ধি বেশিদিন একটানা ফিনিক্সে থাকতে পারতেন না, তাঁকে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষার চেষ্টায় জোহানেসবর্গে আর ভারতবর্ষে দৌড়াদৌড়ি করতে হত। কিন্তু তাঁর পরিবারবর্গ এখানে থাকতেন।
—এখন আর ফিনিক্স ফার্মের জমিজমা নেই,— যেতে যেতে অরিন্দম বললেন কিছু জংলা ঝোপঝাড়ে ভরা পতিত জমি দেখিয়ে,–এই সবই তো গান্ধিজির কেনা জমি ছিল, সে জমির সিংহভাগই সরকার অধিগ্রহণ করে ফেলে রেখেছে, এই পাঁচিল ঘেরা বাড়িঘরটুকু ফিনিক্স ট্রাস্টের আছে। মণিলাল গান্ধির মেয়ে ইলা এখনও ট্রাস্টের দায়িত্বে আছেন।
প্রাচীরে ঘেরা অঞ্চলটিতে প্রবেশের মুখেই বাইরের দিকে সবার আগে চোখে পড়ে মস্ত করে নাম লেখা দেওয়ালে, ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট প্রিন্টিং প্রেস,১৯০৩। সেই সব প্রাচীন প্রিন্টিং প্রেসের কাঠের যন্ত্রপাতিগুলি এখনও সযত্নে রক্ষিত আছে, যেগুলি দিয়ে স্বহস্তে পত্রিকা বের করতেন গান্ধি ও তাঁর সহকর্মীরা। হাতার ভিতরে ঢুকে— প্রথমে রয়েছে কস্তুরবা গান্ধির নামে শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ক্লিনিক। বাগানের ভিতরে একটি ঝকঝকে নতুন বাংলো বাড়ি, সেটি একদা ছিল মণিলাল গান্ধির বাড়ি, এখন সেখানে লাইব্রেরি। আজ বন্ধ। প্রেসও বন্ধ। ক্লিনিক, প্রাইমারি স্কুল সবই বন্ধ থাকে শনি-রবিবার। আজ ভুল দিনে এসেছি।
একসময়ে আগুন লাগিয়ে গান্ধির ঘরবাড়ি, সর্বোদয় আশ্রম, সব কিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে লণ্ডভণ্ড করে দেওয়া হয়েছিল। মণিলাল গান্ধির বাড়ি পুরো পুড়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, নতুন করে তৈরি হয়েছে। একটু ওপাশে নেমে, সর্বোদয় আশ্রম নামের ফলক লাগানো গান্ধিজির নিজস্ব বাড়িটিতে শুধু পাথরের তৈরি পুরনো সিঁড়িটা অক্ষত আছে। বাকিটা ভস্মীভূত হবার পরে পুনর্নির্মিত তবে অবিকল আগের মতো। কাঠের, শূন্য, চাকচিক্যহীন। ঢুকে সবরমতী আশ্রমের ঘরের কথা মনে পড়ে গেল। একই ধরনের। শুধু এখানে কোথাও কোনও চরকা নেই। থাকার কথাও না। ব্যবহৃত কোনও আসবাবও কিন্তু দেখলুম না। ফলে বসতবাড়ির চেহারা আর নেই, জাদুঘরের মতো দেওয়ালে টাঙানো আছে প্রচুর ছবি, চিঠিপত্র, গান্ধির দক্ষিণ আফ্রিকার জীবনের ইতিহাস। বুঝতে পারছি সেই সময়ে ফিনিক্স ফার্মের স্পর্শ এখন এখানে কিছুই পাওয়া যাবে না আর, তবু এই ঘরে এই ছবিগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে গায়ে কাঁটা দেয়। দেশ থেকে কত দূরে এসে একজন মানুষের তরুণ হৃদয়ে পরাধীনতার অপমানবোধ তীব্র হয়ে বেজেছিল, সেই স্বদেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখা শুরু। অরিন্দম বললেন, ওড়িশার এক কংগ্রেসি মন্ত্রী নাকি এখানে এসে অঝোরে কেঁদেছিলেন।
বেরুনোর পথে দেখি একগুচ্ছ নীলবসনা কৃষ্ণাঙ্গিনী নারী। হঠাৎ দেখলে ক্রিশ্চান সন্ন্যাসিনী মনে হয়, কিন্তু অন্যরকমের সাজসজ্জা। ওরা কারা? অরিন্দম বললেন ওরা শাম্বে স্কুল অফ থট-এর পাস্টর, গ্রামে ঘুরতে বেরিয়েছেন, পাশেই ওদের আস্তানা। ফরাসি মিশনারিদের প্রভাবে তৈরি এই বিশেষ ধর্মীয় দলটি ক্রিশ্চানিটির সঙ্গে সঙ্গে জুলুদের ধর্মীয় আচার, ট্রাইবাল রিচুয়াল্স, সামাজিক রীতিনীতি বেশ কিছু বজায় রেখেছে। ট্রাইবাল আইডেন্টিটি পুরোপুরি বিসর্জন দিতে হয় ওদের। সুন্দর একটা মধ্যপথ আবিষ্কার করেছেন এই উদার শাখা, শাম্বে স্কুল অফ থট। একটা জাতির পুরনো নিজস্ব সংস্কৃতি হোক তা লৌকিক, হোক তা মৌলিক বিদেশি সংস্কৃতির চাপে তাকে মুছে ফেলা মহা অপরাধ। আমেরিকার দুই মহাদেশেই ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকেরা গিয়ে পড়ে সেই মার্জনাহীন অপরাধ ঘটিয়েছিল, স্থানীয় মানুষদের স্বকীয় সভ্যতা নির্দয়ভাবে বিনষ্ট করেছিল, সেকথা ভাবতেও লজ্জা করে। শুনেছি আফ্রিকাতে কিন্তু আরো কোনও কোনও জায়গায় স্থানীয় লোক সংস্কৃতির সঙ্গে মিশনারিরা ক্রিশ্চানিটির সহজ সংমিশ্রন ঘটিয়েছেন যাতে মানুষগুলির নিজস্ব মাটির সঙ্গে সম্পর্কের উচ্ছেদ না হয়ে যায়।
পিটার মারিৎসবর্গ
তবে গায়ে কাঁটা আরো ঢের বেশি দিল তার পরে। সহস্র পাহাড়, তরঙ্গিত শ্যামল শৈলশ্রেণি থাউসেণ্ড হিল্স পেরিয়ে আমরা যখন চলে এলুম নাটালের রাজধানী পিটার মারিৎসবর্গে। নাটালের রাজধানী এখন ডারবানে নেই, মারিৎসবর্গে সরে এসেছে, যদিও সেটি একটি ছোট শহর। ডারবান বৃহৎ। বড় বড় কোম্পানির অফিসের মূল শাখা, বিদেশি কনসুলেট ইত্যাদি সব সেখানেই। কিন্তু আমাদের মতো ব্রিটিশ রাজত্বে জন্মানো আবেগপ্রবণ ভারতীয়ের কাছে এই ছোট স্টেশনের নামটি অবিস্মরণীয়। আজকালকার ছেলেমেয়েরা যদি এর নাম জানে, তারা হয়তো জানবে গান্ধি সিনেমাটি থেকে পিটার মারিৎসবর্গে গান্ধিজিকে ট্রেন থেকে প্ল্যাটফর্মে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া দিয়েই ছবির শুরু। অথবা জানবে কৌন বনেগা ক্রোরপতির কোনও প্রশ্নের উত্তর হিসেবে। যথা: দক্ষিণ আফ্রিকার কোন স্টেশনে গান্ধিজিকে ফার্স্ট ক্লাস টিকিট থাকা সত্ত্বেও ট্রেন থেকে নামিয়ে হয়েছিল? জোহানসবর্গ/ ডারবান/ পিটার মারিৎসবর্গ? দিবি ভাল প্রশ্ন, না?
আমরা যখন পিটার মারিৎসবর্গের স্টেশনে পৌঁছোলুম, তখন বিকেল হয়ে গিয়েছে। অন্ধকার নামছে। মস্ত গাড়িবারান্দাওয়ালা রীতিমতো আভিজাত্যপূর্ণ স্টেশন। ঢুকে মস্ত হলঘর। সম্পূর্ণ ফাঁকা। জনশূন্য তো বটেই, আসবাবপত্রও নেই। শুধু অপরূপ একটি কারুকার্যখচিত কাঠের সিঁড়ি উঠে গিয়েছে দোতলাতে। আর বিশাল এক ঝাড়লণ্ঠন দুলছে ছাদ থেকে। গান্ধিজির সময়েও নিশ্চয় ছিল এগুলি। এরা সাক্ষী আছে তাঁর অপমানের। পাশেই দুটো বন্ধ কাচের দরজায় গায়ে লেখা ওয়েটিং রুম। কাচের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে বেঞ্চি কয়েকটি। দক্ষিণ গোলার্ধের জুন মাসের শীতের রাত্রি গান্ধিজি যেখানে কাটিয়েছিলেন ৭ জুন, ১৯৮৩। ভিতরে দেওয়ালে গান্ধির হাসিমুখ। হাসছেন। হাসবেনই তো।
ভিতরে যাওয়া যাবে? যাবে, চাবি আনলে। ড্রাইভার গেলেন চাবির সন্ধানে, ধরেও আনলেন এক দ্বারপালিকা মহিলাকে। তিনি দোর খুলে দেখিয়ে চলে গেলেন। ঢুকে ছবিটার কাছে গিয়ে দাঁড়াই। তার পরে বেঞ্চে একটু বসি।১৮৯৩-এর জুন মাসটার কথা ভাবতে চেষ্টা করি। দক্ষিণ গোলার্ধে তখন শীতকাল। খুব নাকি ঠাণ্ডা ছিল সেদিন রাতে। গরম জামাকাপড় মালপত্রের সঙ্গে ট্রেনে বয়ে গিয়েছিল। খুব শীত করেছিল ভারতীয় যুবকটির। প্রথম শ্রেণীর টিকিট হাতে থাকা সত্ত্বেও তাকে টেনে নামিয়ে দিয়েছিল রেলের পুলিশ, পাথরের প্লাটফর্মের ওপরে। একজন সাদা সহযাত্রীর অভিযোগে। কালা আদমির সঙ্গে একত্রে তিনি ভ্রমণে রাজি নন। টিকিট থাকা না থাকা অজরুরি, সেই যাত্রীর অপরাধ, সে ভারতীয়। তার রং কালো।
আস্তে আস্তে প্ল্যাটফর্মের দিকে এগোনো যাক। অরিন্দমের সঙ্গে সেইখানে গিয়ে দাঁড়াই যেখানে একটি কাঠের বেদিতে একটি ফলকে লেখা রয়েছে, ৭জুন ১৮৯৩ এর দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা থেকেই শুরু হয়েছিল গান্ধির অ্যাকটিভ নন ভায়োলেন্সের নীতি। কিন্তু লেখা নেই যে ওঁর হাতে প্রথম শ্রেণির টিকিট ছিল। শুধু প্রথম শ্রেণি থেকে নামিয়ে দেবার কথাটুকু আছে। কেন যে নামানোটা অনুচিত হয়েছিল সেটা কোথাও লিখিত নেই। এ কথা শুধু ভারতীয়রাই জানবে। অজ্ঞ জনে ভাবতেই পারে, নামিয়ে দিয়েছে যখন, ভদ্রলোক বিনা টিকিটে যাচ্ছিলেন নিশ্চয়! আর অ্যাকটিভ নন ভায়োলেন্সের সঙ্গে প্যাসিভ রেসিস্ট্যান্স শব্দটা থাকলে ভাল হত, এদেশে যখন শব্দটা ম্যাণ্ডেলার নিজস্ব ব্র্যাণ্ড মার্কা হয়ে গিয়েছে। স্বত্বাধিকারী নামটা বিশেষ কেউ জানে না।
এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণগিরি। সেখান থেকে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের আত্মশক্তির এক নবীন ধারাস্রোত উৎসারিত হয়েছিল। আমি একটু অন্যমনস্ক ছিলুম হঠাৎ আমাদের কনসুলেটের গাড়ির মধ্যবয়স্ক কালো আফ্রিকান ড্রাইভার মারভিন আপন মনে বলে ওঠে, ‘যততোবার আমি এখানে আসি, অনেকবার তো এলাম, প্রতিবার গায়ে কাঁটা দেয়।’ আমি স্তব্ধ হয়ে তার দিকে চেয়ে থাকি। ও বলে যায়, ‘আমি একা নই। ইণ্ডিয়ার প্রাইম মিনিস্টারও এখানে দাঁড়িয়ে অবিকল তাই-ই বলেছিলেন। গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। বলেছিলেন, এখানে একটা বিশেষ পরিমণ্ডল অনুভব করা যায়। রোমাঞ্চ হয়।’
—মনমোহন? অরিন্দম বলে,—হ্যাঁ, উনি এসেছিলেন।
এর পরে আমার আর আলাদা করে বলার কিছু রইল না। এই আফ্রিকার ছেলেটি আমার মনের অনুভূতিটুকু প্রকাশ করে দিল তার নিজের মনের ভাষাতে।
অরিন্দম বললেন, চলুন দিদি পিছনে স্টেশনের সাইনবোর্ডটা দিয়ে আপনার আর অনির্বাণের একটা ছবি তুলে রাখি। এখন অবশ্য নাম বদল হয়ে হয়েছে মুসুম দুজি। পুরনো সাইনবোর্ড রয়েছে।
—আমাকে ই-মেল করে দিয়ো কিন্তু ছবিগুলো।
—নিশ্চয় দেব।
কিন্তু আমি জানি কেউ দেয় না। আমি চলে গেলেই কাজের চাপে অরিন্দম সম্ভবত ভুলে যাবেন, তাই আমি আমার ক্যামেরাতে, যদিও সে নো ব্যাঁটারি দেখাচ্ছে, তবু দুটো জবরদস্তি তুলে ফেলি।
–দিদি, এবারে যাবেন?
—চলো না একটু বসে থাকি এই প্ল্যাটফর্মে।
কিন্তু বসা অসাধ্য। প্ল্যাটফর্মে যদিও যাত্রী নেই টিকিটঘর খোলা নেই, কিন্তু বাইরে প্রত্যেকটি বেঞ্চিতে শতচ্ছিন্ন কাঁথা জড়ানো ধুলি মলিন মানুষ শুয়ে আছে, এই বিকেলবেলায়। দীন দরিদ্র এবং নেশাগ্রস্ত, অচেনা কিছু নারী ও কিছু পুরুষ। সকলেই কালো। একটিও আসন ফাঁকা নেই। বসার কোনও জায়গা ছিল না। জায়গা থাকলেও অরিন্দম বসতে দিতেন না ওদের মধ্যে। সাহস পেতেন না। এখানে ক্রাইম রেট জোহানেসবর্গের চেয়ে কম হলেও যথেষ্ট বেশি। প্ল্যাটফর্মের এই স্মরণযোগ্য দৃশ্যটার ছবি তোলার ইচ্ছে হলেও রুচি হল না। সাহেবদের কলকাতার বস্তির ছবি তোলার মতো হত। মন থেকে এ ছবি মিলিয়ে যাবার নয়।
পরবর্তী গন্তব্য, এই শহরের কেন্দ্রে স্থাপিত গান্ধির সেই দীর্ঘ মার্চের মূর্তি দর্শন। শুনলুম এখানে ম্যাণ্ডেলার একটি মূর্তি বসানোর কথা হচ্ছে সত্যাগ্রহের একশো বছর পূর্তি উপলক্ষে। ম্যাণ্ডেলা তাঁর আত্মজীবনীতে (দ্য লং মার্চ টু ফ্রিডম) লিখছেন, গান্ধির প্যাসিভ রেসিস্ট্যান্স পদ্ধতি ছাড়া উনি প্রতিবাদের আর কোনও পন্থা খুঁজে পাচ্ছিলেন না।
ফেরার পথে একটা বিজ্ঞাপন দেখে অনির্বাণ খুব বিচলিত। এখানেই কোনও এক করেসপণ্ডেস বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞাপন সে দেখে পোস্টারে গান্ধির ছবি আর একজন সাদা মানুষ তার পিছনে যেন তাকে পেট্রোনাইজ করার ধরনে দণ্ডায়মান ব্যাপারটা কী। তবে দিল্লির কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রের আপত্তিটার একটা ওজর আছে বৈকি।
হঠাৎ অনির্বাণের মন ভাল হয়ে গেল। আন্টি, দ্যাখো দ্যাখো কী সুন্দর একটা রামধনু। এত বড় আর এত পরিষ্কার। সবগুলো রং যেন আলাদা আলাদা দেখা যাচ্ছে, দেশে কক্ষনো এমন সুন্দর রামধনু দেখিনি। সকলেই রামধনু আর তার রং ব্যবহার দেখতে পেলেন, আমি ছাড়া। অত দূরের জিনিস কাছে সন্ধ্যার আলো-আঁধারিটাই বড় হয়ে রইল। তবু যা দেখেছি সে-ই অনেক। দেখতে তো পাচ্ছি এখনও। হাতের কাছে কোলের কাছে যা আছে তা অনেক আছে।
–আচ্ছা, গান্ধির নামে এখানে কোনও রাস্তা টাস্তা নেই? কোনও পার্ক স্কোয়ার?
—আছে, সম্প্রতি ডারবানের পয়েন্ট রোড নাম পাল্টে মহাত্মা গান্ধি রোড করেছে। তাতে ভারতীয়রা খুব বিরক্ত।
—বিরক্ত? কেন?
–কেননা পাড়াটা খুব খারাপ, ডকের পাড়া, ভীষণ ক্রাইম রেট বেশি ওখানে এবং বেশ্যাপল্লি, তারা সন্ধ্যায় সারি দিয়ে পথে দাঁড়িয়ে থাকে। মহাত্মা গান্ধির জন্যে ঐ রাস্তাটা ছাড়া কি গোটা শহরে আর রাস্তা ছিল না?
–বাড়ি ফেরার পথে একবার ঘুরিয়ে বরং মহাত্মা গান্ধি রোড। সবগুলি গান্ধি স্মৃতি-বিজড়িত স্থান-ই দেখে যাই। যথাসাধ্য।
তাই হল, একটি রাস্তায় গেলুম। তার খানিকটা আলোকিত, দিব্যি বড় বড় দোকানপাট আছে, আর ডকের দিকে খানিক অংশ নিরালোক। হঠাৎ দেখি দুটি নেহাত অল্পবয়সী কিশোরী কৃষ্ণাঙ্গী মেয়ে আপনমনে নাচতে নাচতে বিপজ্জনকভাবে চলন্ত গাড়ির সামনে দিয়ে রাস্তা পার হচ্ছে, স্পষ্টতই মত্ত। আমার মনে পড়ে গেল, ১৫ থেকে ২৫ বছরের মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছড়িয়ে পড়েছে এইচ-আই-ভি এইডসের মৃত্যুবীজ। প্রধান কারণ জলদি দু পয়সা করে নেওয়ার লোভ।
অরিন্দম দেখালেন- ঐ যে দিদি।
দেখলুম রাস্তার মোড়ের মাথায় দুটি ফলক লাগানো, ওপরে পুরনো নাম, পয়েন্ট রোড এবং তার নীচে নতুন পরিচয় এম কে গান্ধি রোড।
—ওরা প্ল্যান নিয়েছে এরিয়াটি একেবারে বদল করে ফেলবে। আগে থেকেই তাই এই নাম। দুর্ভাগ্য পল্লির শুদ্ধিকরণের শুরু।
পরে কেপটাউনে এসে নাটালের এম পি শ্রী মেওয়া রামগোবিনের মুখে শুনলুম, তাঁর মতে, এই পুণ্য নামের মাহাত্ম্য ঐ হিংসাজর্জর অপরাধপ্রবণ অঞ্চলটি ক্রমশ অহিংস ও পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠবে, এটাই নগরোন্নয়নের অধিকর্তাদের আশা। তাঁরা সেই মর্মে চেষ্টা চালাবেন। মেওয়া রামগোবিন্দ একদা মণিলাল গান্ধির কন্যা ইলা গান্ধির স্বামী ছিলেন। ওঁদের চার সন্তান। মেওয়া সগর্বে বলেন, তাঁর পূর্বপুরুষ এসেছিলেন বিহার থেকে আখের খেতের চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হয়ে। ইলা এখনও ডারবানে ফিনিক্স ফার্মের ট্রাস্টি। রামগোবিন আবার বিবাহ করেছেন, অনেক বয়ঃকনিষ্ঠ এক মুসলিম কন্যাকে। সে ডারবানেরই গুজরাটি বণিক পরিবারের ১৪তম সন্তান, মরিয়ম। তাঁরা বাস করেন কেপটাউনে, দক্ষিণ আফ্রিকার পার্লামেন্ট সেখানেই। তাঁদের এক কলেজে পড়ুয়া ছেলে। মরিয়মের আগের বিবাহের একটি মেয়ে আছে। সে এখন বিবাহিত। মরিয়মের গল্পটাও অসাধারণ।
অরিন্দম ধললেন— দিদি, একদিন থাকলে কি কিছু হয়? ডারবানে গান্ধিজি যে স্টেশন থেকে ঐ ট্রেনে উঠেছিলেন, সেই ওল্ড স্টেশন বিল্ডিংয়েই আমাদের ইণ্ডিয়ান কনসুলেটের অফিস। সেটা তো দেখার সময় পেলেন না? সেখানেও কিন্তু গান্ধিজির মূর্তি আছে। আর নিচেই টুরিজম -এর অফিস। অনেক দরকারি ইনফর্মেশনের কাগজপত্রও পেতেন, কিন্তু এটা শনি রবিবার। সব বন্ধ! তার চেয়ে চলুন এবারে আপনাকে ব্লু লেগুনে নিয়ে যাই। শনি রবিবারেই সেখানে সবাই যায়।
ব্লু লেগুনে? সে আবার কী? সে তো একটা সিনেমার নাম।
—সিনেমা নয়। বীচ। ইণ্ডিয়ানদের বীচ।
–সে কি, এখনও আলাদা আলাদা বীচ?
—এখন আর আলাদা নেই, সবই ওপেন টু অল, তবু ঐ ইণ্ডিয়ান পাকিস্তানিদের এটাই বেড়াবার জায়গা। নিজেদের মতো করে একটু রিল্যাক্সড করে থাকতে চায় সকলে। সাদাদের বীচ, কালোদের বীচও আছে এখানে। তবে কালোরা এখন সাদাদের বীচেই যাওয়া পছন্দ করে বেশি। নিষিদ্ধ ছিল তো। চলুন না নিজেই দেখবেন।
মোহনা • মৎস্যশিকারী • সস্তায় কিস্তিমাত
পিটার মারিৎসবর্গ থেকে ফিরে সোজা আমরা সদলবলে হাজির হলুম ডারবানের সমুদ্রতীরে। সমুদ্রতীরের আগেই একটি জায়গা দেখে আমার মনে হল আরে, এটা তো চৌপাট্টি বাঁধানো পাঁচিলের ধারে পাশাপাশি নানা রকমের ফাস্টফুডের খুদে তাঁবু, আর অনেক কিছু জাংক বিক্রি হচ্ছে, চুলের ক্লিপ, বোতাম, প্লাস্টিকের ফুল, প্লাস্টিকের গয়না, টি শার্ট, ছোটদের খাতা, রঙিন, পেনসিল, প্লাস্টিকের খেলনা, সস্তা দুল চুড়ি। কলকাতার ফুটপাথের বাজারের মতো অনেকটা, অপারেশন সানসাইনের আগে ছিল রাস্তাঘাটে রিফিউজিদের দোকানপাট, ঠিক যেন মেলা বসেছে। বড় বড় গাড়ি পার্ক করা, চতুর্দিকে কল-কাকলি, ভারতীয় দর্শনা বাচ্চারা ঘুরছে মায়ের হাত ধরে বাবার হাত ধরে, আইসক্রিম খাচ্ছে, দোসা, বড়া, ইডলি খাচ্ছে ভুট্টার সেদ্ধ দানা মাখা চাট খাচ্ছে, ঠিক ঝালমুড়ির মতো করে। আমি তো লোভী, দেখেই বলেছি, আমরা খাব না ঐসব? অরিন্দম যারপরনাই বিব্রত। ম্যাডামের কি যোগ্য খাদ্য এটা? অনির্বাণ অমনি গোঁ ধরেছে, ইয়েস ইয়েস, আমিও খাব আন্টি, মি টু। অতএব আমরা বীরগর্বে দুজনে দুপাতা (কাগজের প্লেটে) ভুট্টা চাট নিলুম, অনেক রকমের টক ঝাল, মিষ্টি আচার ও সস, এবং চাটনি পাশে রাখা আছে, নিজের খুশিমতো মেখে নাও। আমার মাখাটা অপূর্ব হল, আমি খুব মজা করে খেলুম। অনির্বাণ বেচারা ভাল করে চাটনি মাখেনি। তাই ওর মনে হল দিল্লির ভুট্টা বেটার।
পাশে একটা মোটামুটি রোগামতো নদী বইছে, তার নাম উঙ্গেনি। বাঁধানো বেঞ্চির মতো পাড়ে সারি সারি ছিপ ঝুলিয়ে আশার ছলনে ভোলা মানুষেরা বসে আছেন। ছলনা নয়, বেশ ভালই মাছ ওঠে, অরিন্দম বলেন। এরা এসেছেন হোল নাইটের প্রোগ্রামে। সারা রাত্রি মাছ ধরবেন। শনিবার রাত্রি আজ। এটা এখানে রেওয়াজ। আমরা হাঁটছি উঙ্গেনি নদীর পাড় দিয়ে, সুন্দর সন্ধ্যার বাতাস দিচ্ছে, কিন্তু ফেরিওয়ালাদের সে কি উৎপাত। মোজা জুতো সিডি, ডিভিডি সব খুব সস্তা লেটেস্ট বম্বে ছবির গান এবং সিনেমা। ফিরিওয়ালারা সবাই ভারতীয় নন, পঞ্চাশ ভাগই পাকিস্তানি আর বাংলাদেশি। এদের মধ্যে আফ্রিকান দেখা গেল না। শুনলুম এঁরাও পুলিশ এলে লুকিয়ে পড়েন। ফ্রান্সে, ইটালিতে জার্মানিতে একই দৃশ্য দেখেছি ছুটে পালাবার। প্রায় সকলেই ইল্লিগাল ইমিগ্র্যান্ট, বেআইনি ব্যবসায় লিপ্ত। অনির্বাণ সদ্য উদ্বোধন হওয়া প্রোভোকড্ -এর ডিভিডি দেখে কিনতে চাইল, বাবা বললেন, এখানে নিয়ো না, না চললে বদল হবে না। এ তো সবই চোরাই। এখনও এর ডিভিডি রিলিজ করেনি। অনেক সময়ে এগুলো টিভিতে চলে না। ছেলে বললে টিভিতে না চলুক, কম্পিউটারে চলবে। কিন্তু আপাতত বাবার পরামর্শই রইল। আমরা হাঁটতে হাঁটতে মোহনার দিকে, সমুদ্রের দিকে যাচ্ছি আসল বীচে পৌঁছব। এটা তো বীচ নয়। উঙ্গেনি নদীর তীরে। এখানে সমুদ্রও নেই বালুকাবেলাও নেই, কিন্তু খুব সুন্দর। নদীর ওপারে কিছু দেখা যাচ্ছে না। শান্ত, নির্জন অন্ধকার। অল্পস্বল্প আলো দূরে মিট মিট করে জ্বলছে, নিচু তারার আলোর মতন। রাত্রি নেমে এসেছে। ভীড় সব এপারে। এই জায়গাটি সবটাই অবশ্য ল্যাগস, ব্লু লেগুনের এই আদুরে ডাকনামে ভারতীয়দের মধ্যে চালু বিপাশা বসু যেমন বিপস। হঠাৎ আমার পা আর চোখ একসঙ্গে থমকে দাঁড়াল। দেখি সামনে আশ্চর্য এক দৃশ্য। বিশাল বড় বড় উঁচু কালো ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছে রোগা নদীটার সরু মুখে। অনেক দূর পর্যন্ত নদীর বুকের ভিতরে উজান বেয়ে জোর করে ঢুকে আসছে সাদা ফেনার ফণা তোলা দুর্ধর্ষ কালো জলের তরঙ্গ, নদীর শান্ত স্রোতের বিপরীতে সমুদ্রে এসে গিয়েছে। সমুদ্রে জোয়ার আসছে, কৃশকায়া উঙ্গেনি নদী কখন তার ঘরে আসবে তার তোয়াক্কা না করে। শুনে এসেছি এতকাল, নদীরাই গিয়ে সমুদ্রের বক্ষে আছড়িয়ে পড়ে, মোহনাতে মিলিয়ে যায়। এ তো উল্টো-পুরাণ। সমুদ্রই নদীর বুক ভরে দিচ্ছে। তাড়াতাড়ি ডেকে দ্যাখালুম অরিন্দমকে, আমি তো এরকম আশ্চর্য সুন্দর প্রাকৃতিক ঘটনা আগে দেখিনি। অরিন্দম অবাক হলেন না। কিন্তু অনিবার্ণ আমার মতোই চমকৃত হল। আর এই ডারবানের ঊষ্ণ বীচে তো যে সে সমুদ্রের নয়, স্বয়ং ভারত মহাসাগরের তরঙ্গময় আসা যাওয়া। ভারত মহাসাগর! নামটি শুনেই হঠাৎ বুকের মধ্যে ঘুর ঘুর করে উঠল, সেই ছোটবেলার মতো আমার মনে হল, এই একই সমুদ্র তো আমার দেশের মাটিকেও ছুঁয়ে আছে, এই জলে আমার দেশেও হাত ছোঁয়াতে পারব, তা হলে আর আমি দেশ থেকে এমন কী দূরে?
অরিন্দমের কথাই ঠিক, সাদাদের বীচে শুধুই কালোদের সপরিবারে আনাগোনা দেখা দেয়। সমুদ্রতীরে জুয়ার আড্ডা পশ্চিমী জগতের এক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। ইউরোপে আমেরিকায় সর্বত্র আছে, এখানেও তার ব্যত্যয় নেই। কাসিনো রয়েছে। সাহেব বিবিদের দেশে উঁচু পর্বতের চূড়োয় উঠলে দেখবেন ঠিক একটা পাব, একটা কফিশপ আছে, আর আমাদের দেশের পাহাড়ের চূড়োতে উঠলেই একটা মন্দির। আমরা আর নামিনি কোথাও। আমাদের নৈশভোজের সময়ের বিলম্ব হয়ে যাচ্ছিল, সোজা অরিন্দমের বাড়িতে ছুট। অনেক নিমন্ত্ৰিত মানুষ এসে বসে থাকবেন নইলে।
টাকডুম টাকডুম বাজে বাংলা মায়ের ঢোল
যতজন বঙ্গসন্তানকে ডাকা সম্ভব হয়েছিল এই অল্প সময়ের নোটিশ, অরিন্দম সকলকেই ডেকেছিলেন সেই নৈশভোজে। খুব মন ভাল লাগে যখন পৃথিবীর এত সুদূর প্রান্তেও চেনা মুখের দেখা পাই। চেনা মুখ, কেননা তাঁরা আমার লেখার মধ্য দিয়ে আমাকে চিনে ফেলেছেন। কথাবার্তাতে অনেক কমন রেফারেন্স উঠে আসে। ডিনার ভারতীয়, এখানকার ভারতীয় রেস্তোঁরা থেকে আনানো অগুন্তি পদবৈচিত্র্য। কিন্তু রান্নাটা একটু অন্য রকমের। অনেক ঘি, কাজুবাদাম বাটা ইত্যাদি আছে সর্বত্র, ঠিক বাঙালি রসনার উপযুক্ত কি? সে যাই হোক, মাছ, মাংস, পনির সব কিছু ছিল। ভাল দার্জিলিং চা-ও ছিল; খুব সুন্দর বাঙালি আড্ডা হল। ডারবানে ঐ একটি নিশীথে।
পরের দিন সকালেই কেপটাউন রওনা। হর্ষ, হর্ষের বাবা মা এবং হর্ষের স্ত্রী ঘরের মেয়েদের মতো করে যত্ন করলেন আমাকে। পরিবারের সকলেই যে খুব আপন করে নিয়েছিলেন আমাকে, সেটা অনুভব করলুম বিদায় নিয়ে রওনা হবার সময়ে
আপন করে নেবার একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে বোধ হয় ডারবানের। সেটা বুঝিয়ে দিল ডারবান এয়ারপোর্টের একটি তরুণ কর্মী। পরের দিন সকালে অরিন্দম পৌঁছে দিয়ে গেলেন, এয়ারপোর্টে একটি মাথা কামানো, ইয়ুল ব্রাইনার টাইপের যুবকের হাতে আমাকে সঁপে দিয়ে তিনি অফিসে ছুটলেন। এই ছেলে জানালে সে যাবতীয় ভিআইপি যাত্রীদের সহায়তা করে। আমার যাত্রার সব বন্দোবস্ত করে আমাকে বিজনেস ক্লাস লাউঞ্জে বসিয়ে হাতে সকালের কাগজ, কফি, কমলার রস ও কাজু দিয়ে বলে গেল সময়মতো এসে আমার চক্র -যানটি প্লেনে নিয়ে যাবে।
—আপনার নাম?
—কানহাইয়া। উই কেম ফ্রম বিহার মেনি জেনারেশনস আগো। একমুখ হাসেন কানহাইয়া। বাট উই হ্যাভ ফরগটন হিন্দি।
আবার এক একটি করে হুইল চেয়ার প্লেনে উঠছে সেই লিফটের গাড়িতে। দুজনে উঠে গেলেন। আমাকে কানহাইয়া গাড়িতে তুলে দিতেই অকস্মাৎ গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে লিফটের ছোকরাটি আমার চক্র-যানটি প্লাটফর্ম থেকে ঠেলে আবার মাটিতে নামিয়ে দিল। বলল,—নো সার, নট শি।
বেশ সুন্দর শ্যামলা মুখখানি, চুলে ঝুঁটি বাঁধা কানে মাকড়ি। চেহারা দেখলে তো ভালই লাগে কী হল রে বাবা?
কানহাইয়াও ঘাবড়ে গিয়ে বলল–হে হোয়াটস দ্য ম্যাটার?
ছেলেটি ভুরু কুঁচকে বলে,
—শি কেম টু ডারবান ওনলি ইয়েস্টারডে মর্নিং অ্যাণ্ড শি ইজ লীভিং টুডে মর্নিং। উই ক্যান নট অ্যালাউ দিস। ক্যান উই, কানহাইয়া? শি মার্স্ট স্টে অন ফর আ উইক অ্যাট লিস্ট। আই শ্যাল নট পুট হার ব্যাক অন দিস প্লেন!
সবাই হো হো করে হেসে ওঠে, ছেলেটিও আমাকে লিফটে তুলে নেয় নিজেই। আর ঘন ঘন মাথা দুলিয়ে বলে,—দিস ইজ আনফরগিভেবল ম্যাডাম! কামিং টু ডারবান ফর আ ডে অল দ্য ওয়ে ফ্রম ইণ্ডিয়া! ছেলেটির আত্মীয়সুলভ অভিমানে মনপ্রাণ ভরে গেল।
-তোমার নাম কী বাছা?
– সাব্বির, ম্যাডাম।
—তুমিও কি ভারত থেকে?
–আমি না, আমার প্রপিতামহ এসেছিলেন গুজরাট থেকে।
—বণিক?
—এখন আমাদের মুদির দোকান আছে, কিন্তু তখন মজুর হয়ে এসেছিলেন।
দরজা বন্ধ হবার মুখে আমার হাত নিজের হাতে নিয়ে আবার একমুখ দুষ্টু হাসির আলো ছড়িয়ে সাব্বির বলে,—হ্যাভ আ গুড টাইম ইন কেপটাউন, বাট দিস ওন্ট ডু, ইউ মাস্ট কাম ব্যাক টু ডারবান!
আমিও বলি,—ইয়েস, সাব্বির, আই মাস্ট কাম ব্যাক!