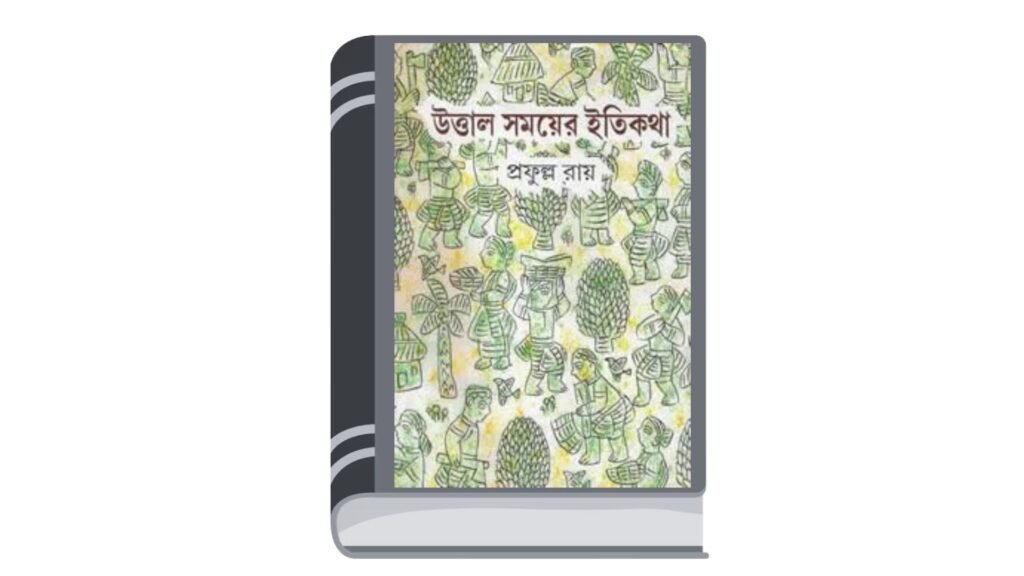৪.১৫ শেখরনাথকে অমান্য করার ক্ষমতা
৪.১৫
শেখরনাথকে অমান্য করার ক্ষমতা জেফ্রি পয়েন্টের উদ্বাস্তুদের কারও নেই। বৃন্দাবন আর মায়ার ব্যাপারে তিনি সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন কেউ যেন ওদের উত্যক্ত না করে। কিছুদিন নিষেধাজ্ঞাটা তারা মুখ বুজেই মেনে নিয়েছে, অনেকটা নিরুপায় হয়েই। কিন্তু ঘৃণা যেখানে প্রবল, কতদিন আর চুপচাপ থাকা যায়। উদ্বাস্তুদের ধারণা, শেখরনাথ ঠিক করেন নি। স্বামীত্যাগী একটি মেয়েমানুষ এবং যে তাকে ফুসলে নিয়ে এসেছে তাদের আশকারা দেওয়াটা খুবই অনুচিত কাজ। এটা জেফ্রি পয়েন্টবাসী ছিন্নমূল মানুষগুলোর কাছে একটা যারপরনাই খারাপ দৃষ্টান্ত হয়ে রইল। কিন্তু কার ঘাড়ে ক’টা মাথা যে শেখরনাথের মুখের ওপর কথা বলে!
আবহাওয়াটা থমথমে হয়েই ছিল। যে কোনও সামান্য ছুতোনাতায় একটা বিস্ফোরণ যে ঘটে যাবে সেটা বৃন্দাবন আর মায়া বুঝতে পারছিল। পুনর্বাসন দপ্তরের কর্মচারী, অফিসার আর শেখরনাথকে বাদ দিলে আর কেউ যে তাদের পাশে নেই সেটা পদে পদে ওরা টের পাচ্ছিল। জেফ্রি পয়েন্টের প্রায় সব উদ্বাস্তু তাদের শত্রুপক্ষ। এই চক্রব্যুহে তারা মুখ বুজেই থাকে। সরকারি কর্মচারী বা শেখরনাথের জন্য কেউ তাদের ওপর হয়তো চড়াও হবে না; কিন্তু কেউ যদি তাদের সঙ্গে কথা না বলে, তাদের শুনিয়ে শুনিয়ে নিজেদের মধ্যে চোখা চোখা মন্তব্য করে যায়, এই নির্বান্ধব পরিবেশে তারা থাকবে কী করে? যথেষ্ট বারুদ মজুদ হয়েই ছিল। শুধু ছোট্ট একটা আগুনের ফুলকি এসে পড়ার অপেক্ষা। আজ সেই ফুলকিটাই এসে পড়ল। তার ফলে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেল।
সকালবেলা চা রুটি টুটি খেয়ে যে উদ্বাস্তুরা তাদের ভাগের জমি পেয়ে গেছে তারা নিজের নিজের জমিতে কাজ শুরু করে দিয়েছিল। কাজ বলতে আগাছা, ঝোঁপঝাড়, পুরনো গাছের শিকড়-বাকড় উপড়ে ফেলা। প্রায় সবার জমিতেই জলডেঙ্গুয়ার (বনতুলসী) চাপ-বাঁধা জঙ্গল; সেসব সাফ করা। এইসব জলডেঙ্গুয়া কয়েক শো বছর ধরে আন্দামানের মাটিতে ঝাড়েবংশে বেড়ে উঠেছে। উর্বর জমি পেয়ে প্রতিটি বনতুলসী এক মানুষ দেড়মানুষের মতো লম্বা; এদের শিকড় মাটির তলায় তানেক দূর অবধি ছড়িয়ে আছে। জলডেঙ্গুয়ার বংশ নিপাত করতে না পারলে ধান চাষ একেবারেই অসম্ভব।
পুনর্বাসন বিভাগের, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকজন বড় বড় গাছ কাটিয়ে ডালপালা এবং গাছের গুঁড়ি খন্ড খন্ড করে হাতি দিয়ে সরিয়ে ট্রাকে তুলে নিয়ে স’মিলে পৌঁছে দেয়। প্যাডক, চুগলুম, দিদু বা রেনট্রি–এমন সব মহাবৃক্ষের মোটা মোটা শিকড় মাটির তলায় কতদূর চলে গেছে ওপর থেকে বোঝার উপায় নেই। এই সব গাছের শিকড়ও বনবিভাগ থেকে তুলে নিয়ে যায়। বাকি জঙ্গলটা সাফ করতে হয় উদ্বাস্তুদেরই। এ মায়া আর বৃন্দাবন তাদের জমিতে আজ জলডেঙ্গুয়া কাটছিল। পাঁচ একর অর্থাৎ পনেরো বিঘা জমির জঙ্গল সাফ করা কি মুখের কথা! পুনর্বাসনের লোকেরা উদ্বাস্তুদের প্রচুর দড়িদড়া দিয়েছে। বনতুলসী, ঝোঁপটোপ কাটার পর তারা দড়ি দিয়ে সেগুলো বেঁধেছেদে কয়েক খেপে পুবদিকের পাহাড়ের তলায় রেখে আসে। সরকারি কর্তারা ওই এলাকাটাই কাটা ঝোঁপঝাড় রেখে আসার জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অনেকটা জমে গেলে ট্রাকে বোঝাই করে সেসব কোথায় নিয়ে যাওয়া হয় কে জানে।
জমি দেওয়া হলেও এর মধ্যে আল তৈরি করা তো সম্ভব নয়। বাঁশের খুঁটি পুঁতে পুঁতে আপাতত সীমানা ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। আল না থাকায় একজনের জমির ওপর দিয়ে আরেকজনকে যাওয়া-আসা করতে হয়। যতদিন না মাটি কেটে জমির সীমানা বরাবর উঁচু করে আল বানানো হচ্ছে, এইভাবেই যাতায়াত করতে হবে।
বৃন্দাবনদের জমির ঠিক গায়েই মাখন পালদের জমি। দেশে থাকতে মাখন লক্ষ্মী গণেশ সরস্বতী কালী দুর্গা, বছরের কয়েকটা মাস এইসব দেবদেবীর মূর্তি গড়ে বিক্রি করত। কিন্তু এতে ক’টা পয়সাই বা মেলে! তাছাড়া তাতে সাত আটজনের একটা গুষ্টির পেট চলে নাকি? নয় নয়, করেও মাখনের পাঁচপাঁচটা ছেলেমেয়ে, তাছাড়া তারা স্বামী স্ত্রী, বিধবা মা। বছরের বাকি মাসগুলো তো নিষ্কর্মা ঘটের মতো বসে থাকলে চলে না। মাখনদের বেশ কয়েক বিঘে জমি ছিল। যখন মূর্তি গড়ার বায়না থাকত, সেই সময়টা বড় তিনটে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে মাখন চাষবাস করত। তাতে সারা বছরের খোরাকিটা উঠে আসত। বাকি খরচ মিটত মূর্তি গড়ার মজুরি থেকে। মোটামুটি এইভাবেই জীবনের এতগুলো বছর কাটিয়ে এসেছে মাখনরা। কিন্তু দেশভাগের পর এতদিনের অভ্যস্ত জীবন পুরোপুরি পালটে গেছে। ঘরবাড়ি জমিজমা খুইয়ে সীমান্তের এপারে আসতেই তাদের গায়ে লেগে গেল ‘রিফিউজি’ তকমা। বছরখানেক দমদমের ত্রাণশিবিরে কাটিয়ে এখন তারা জেফ্রি পয়েন্টের বাসিন্দা। বংশগত মূর্তি তৈরির যে ধারাটা বাপ-ঠাকুরদা এবং তাদের বাপ-ঠাকুরদাদের আমল থেকে একশো দু’শো বছর কি তারও বেশি সময় ধরে চলে আসছিল, বর্ডারের এপারে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে তাতে চিরকালের মতো ছেদ পড়ে গেছে। আন্দামানে এসে পাঁচ একর অর্থাৎ পনেরো বিঘা জমি পাওয়ার পর মাখনদের চাষবাস ছাড়া আর কোনও গতি নেই; বাকি জীবনটা এই নিয়েই কাটিয়ে যেতে হবে। শুধু তারাই নয়, ছুতোর, কর্মকার, জেলে, বারুই, মল্ল, সকলেরই এক হাল। চোদ্দ পুরুষের বৃত্তি খুইয়ে এখানে আজীবন হয়তো জমিতে লাঙল ঠেলেই চলতে হবে।
আজ সকাল থেকে অন্য সবার মতো মাখন, মাখনের বউ কালী আর তিন ছেলে মেঘু, শীতল আর গাকে নিয়ে অন্য উদ্বাস্তুদের মতো তাদের জমির আগাছা শিকড়বাকড় তুলে দড়ি দিয়ে বিশাল বিশাল একেকটা বান্ডিল বেঁধে খেতের একধারে জমা করে রাখছিল।
ওদিকে বৃন্দাবনদের জমির কোণের দিকে আগাছার বাণ্ডিলের পাহাড়। কম করে চল্লিশ পঞ্চাশটা বাণ্ডিল তো হবেই। জলডেঙ্গুয়ার ঝাড়ে দা চালাতে চালাতে বৃন্দাবনের নজর সেদিকে চলে যায়। একটু দূরে মায়া গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে শিকড়বাকড় তুলছিল। সে তাকে বলল, ‘মায়া, মেলা (অনেক) বোঝা জইমা গ্যাছে। এক কাম করি, এগুলানরে (এগুলোকে) পুবের পাহাড়ে রাইখা আহি (আসি)।
একটানা জমিতে কাজ করে চলেছে মায়া। তার কপালে দানা দানা ঘাম জমেছে। পরিশ্রমে মুখটা লাল টকটকে। হাওয়ায় চুল উড়ছে। শাড়ির আঁচল দিয়ে ঘাম মুছে সে বলল, ‘লও (চল), আমিও তুমার লগে (সঙ্গে) বোঝা লইয়া যাই।
মাথা নাড়তে নাড়তে বৃন্দাবন বলল, না না, এই কাম মাইয়ামাইষের (মেয়েমানুষের) না; তুমি পারবা না। আহো (এসো), আমার মাথায় বোঝা তুইলা দিবা।
মায়া অনেক বোঝালো, দু’জনে বান্ডিলগুলো নিয়ে গেলে কাজটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। কিন্তু কোনওভাবেই রাজি হল না বৃন্দাবন। অগত্যা ধরাধরি করে দুটো বান্ডিল তার মাথায় তুলে দিল মায়া।
বৃন্দাবনকে যেতে হবে মাখনদের জমির ওপর দিয়ে। যখনই সে আর মায়া এইভাবে যাতায়াত করে, মাখনরা তীব্র বিরক্তি এবং ঘৃণায় ভুরু কুঁচকে তেরছা নজরে তাকায়। বুঝিয়ে দেয়, জেফ্রি পয়েন্টের অন্য উদ্বাস্তুরা যতবার খুশি তাদের জমিতে আসুক আপত্তি নেই, কিন্তু বৃন্দাবনদের যাওয়া আসাটা তাদের ঘোর অপছন্দ। পারলে ওদের ছিঁড়ে খায় কিন্তু কিছুই করার নেই। পুনর্বাসন দপ্তরের কর্তারা, বিশেষ করে শেখরনাথ হুশিয়ারি দিয়েছেন কেউ বৃন্দাবনদের সঙ্গে ঝামেলা করলে তার ফল ভাল হবে না। তাই মুখ বুজে, নিঃশব্দে অঙ্গভঙ্গি করেই মাখনদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়।
সনাতনের সঙ্গে সেই ঝঞ্ঝাটের পর মায়া আর বৃন্দাবন নিজেদের পুরোপুরি গুটিয়ে নিয়েছিল। তারা বুঝে গেছে সৃষ্টিছাড়া এই কলোনিতে তাদের বান্ধব বলতে উদ্বাস্তুদের মধ্যে একজনও নেই। নেহাত পুনর্বাসনের অফিসাররা আর শেখরনাথ মাথার ওপর আছেন, তাই কোনওরকমে টিকে আছে।
আজকের দিনটা ভাল ছিল না মায়াদের পক্ষে। মাথার বিশাল বোঝা দুটো দুদিক থেকে দু’হাতে ধরে মাখনদের জমিতে চলে এসেছিল বৃন্দাবন। সে টের পাচ্ছিল, ধারাল বর্শার ফলার মতো মাখনদের সারা গুষ্টির হিংস্র চোখ তার পিঠে একের পর এক বিধছে। সে কোনও দিকে তাকাল না, প্রায় দমবন্ধ করে এগিয়ে যাচ্ছিল, আচমকা একটা বুনো গাছের শিকড়ে ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটা আটকে যাওয়ায় মাথার বোঝাসুদ্ধ হুড়মুড় করে পড়ে গেল। যে দড়ি দিয়ে বোঝাটা আটকানো ছিল সেটা ছিঁড়ে গিয়ে সব শিকড়বাকড় এবং আগাছা ছত্রখান হয়ে মাখনের জমির অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল।
পায়ে বেশ জোরেই লেগেছে। যন্ত্রণায় বুড়ো আঙুলটা ভীষণ টাটাচ্ছে। কোমর আর বুকেও চোট পেয়েছে বৃন্দাবন। আছড়ে পড়ায় চোখের সামনের সমস্ত কিছু অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ অনেকের প্রবল চিৎকার কানে এল। প্রথমটা আবছা আবছা, তারপর খুব স্পষ্ট হয়ে। ডান হাতের ভর দিয়ে ধড়মড় করে উঠে বসল বৃন্দাবন। ততক্ষণে মাখন পালের বিশাল বাহিনী তাকে ঘিরে ধরেছে। সবার চোখমুখ ক্রোধে আক্রোশে গনগন করছে।
হাত-পা ছুঁড়ে মাখন বলছিল, ‘এইডা (এটা) কী অইল (হল)? কী অইল এইডা?’
অন্য সবাই গলার শির ছিঁড়ে চেঁচিয়ে চলেছে। আশপাশের জমিগুলো থেকে উদ্বাস্তুরা চলে এসেছে। মথুর সাহা, হারাধন, খগেন, সৃষ্টিধর–এমন অনেকে। তারাও প্রচন্ড উত্তেজিত। ওধারের জমি থেকে মায়াও এসে একধারে দাঁড়িয়েছে। তার চোখেমুখে ত্রাস, উৎকণ্ঠা। শ্বাসরুদ্ধের মতো তাকিয়ে আছে সে। কী করবে যেন বুঝে উঠতে পারছে না।
পায়ের বুড়ো আঙুলের নখটা ফেটে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে। সেদিকে হুঁশ নেই বৃন্দাবনের। ভয়ে ভয়ে বলল, ‘দ্যাহেন (দেখুন) পালমশয়, আমি কি ইচ্ছা কইরা আপনের জমিনে। শিকড়বাকড় ফালাইছি? নিজেই—’
বৃন্দাবনকে শেষ করতে দিল না মাখন, উন্মাদের মতো হুঙ্কার ছাড়ল।–’ইচ্ছা কইরাই ফালাইছস। তর লাখান (তোর মতো) শয়তান পিরথিমীতে (পৃথিবীতে) আর এট্টা (একটাও) জন্মায় নাই।‘
মাখনের বউ কালীর লকলকে খরসান জিব। তার মতো কোন্দলবাজ (ঝগড়ুটে) মেয়েমানুষ জেফ্রি পয়েন্টে দ্বিতীয়টি পাওয়া যাবে না। চিলের মতো তীক্ষ্ণ গলায় চারপাশের সবার কানের পর্দা চিরে কেঁড়ে চিৎকার করল, কুচরিত্তির, বজ্জাত! য্যায় (যে) পরের বউরে চুরি কইরা আন্ধারমান দ্বীপি পলাইয়া (পালিয়ে) আইতে পারে হ্যায় (সে) আবার কথা কয় কুন (কোন) মুহে (মুখে)?’ রক্তবর্ণ চোখের তারা দু’টো বন বন করে ঘুরছে তার। ডান হাতের আঙুল নাচাতে নাচাতে সে চেঁচাতে লাগল।–’এক্কেরে চুপ মাইরা (করে) থাকবি–’
বৃন্দাবন বলল, ‘চুপ মাইরাই তো থাকি। কিন্তু নিজের চৌখেই তো দ্যাখলেন, ইচ্ছা কইরা ফালাই নাই। তভু আকথা-কুকথা কইতে আছেন ক্যান?’
আগুনখাকির মতো বৃন্দাবনের দিকে তেড়ে গেল কালী এবং তার পেছন পেছন মাখন আর তাদের ছেলেরা। কালী গলার স্বর আরও কয়েক পর্দা চড়িয়ে দিল।–’আকথা কুকথা কী রে? তর (তোর) জিম্ভ (জিব) টাইনা ছিড়া ফালামু—’
হাতের ভর দিয়ে বৃন্দাবন উঠে দাঁড়াল। তার মেজাজও তিক্ত হয়ে উঠেছে। রুক্ষ গলায় এবার বলল, ‘পায়ে পাও বাজাইয়া কাইজা (পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া) করেন ক্যান? আমার ধৈয্য (ধৈর্য) কিলাম থাকতে আছে না।‘
পেছন থেকে সামনের দিকে এগিয়ে এল মাখন। চোখ পাকিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে মুখ ভেংচে বলতে থাকে, ‘ধৈয্য থাকতে আছে না! কী করবি রে তুই হুমুন্দির পুত (সম্বন্ধীর ছেলে), কী করবি তুই!’
অনেকক্ষণ সহ্য করার পর এতক্ষণে রুখে উঠল বৃন্দাবন।–’গাইল (গালাগালি) দিও না পালের পুত। সোম্মান (সম্মান) দিয়া কথা কইতে আছিলাম। এইবার কিন্তুক ছাড়ুম না—’
কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে উঠল মাখন।–’তুই আমার এইটা ছিঁড়বি–’ বলে শরীরের বিশেষ একটা অংশ দেখিয়ে দিল।
এদিকে চিৎকার চেঁচামেচি শুনে কাজকর্ম ফেলে আরও দূরের জমিগুলো থেকে অনেকে চলে এসেছে। মায়া আরও এগিয়ে এসেছিল। সকালবেলায় এমন একটা কান্ড ঘটে যাবে, সে ভাবতেও পারে নি। তবে বুঝতে পারছিল চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। তার মুখটা শক্ত হয়ে উঠছিল।
অন্য যে উদ্বাস্তুরা এসেছে তারা হল জলধর বারুই, মহাদেব রুদ্রপাল, গগন বিশ্বাস, বসন্ত দাস, চন্দ্র জয়ধর এবং আরও অনেকে। তারা বেশির ভাগই বয়স্ক লোকজন। তাদের দিকে তাকিয়ে বৃন্দাবন কাতর মুখে বলল, ‘আপনেরা হোনেন (শুনুন), পালের পুত আমারে কী কয়? এই বিচার হগলে (সবাই) করেন—’
ক্রোধে উত্তেজনায় ফেটে পড়ল মাখন।–’পুঙ্গির পুত, মানুষজন ডাইকা সালিশি মারাও—’
অন্য উদ্বাস্তুদের দিকে ফিরে বৃন্দাবন বলল, ‘নিজেরাই ক’ন, আমি আপনেগো ডাইকা আনছি?’
মাখনও ভিড়টাকে বলল, ‘উই দ্যাহেন (ওই দেখুন) হালার পুতে আমার জমিনে শিকড়বাকড় ফালাইয়া কী করছে! আমি অরে (ওকে) গাইল (গালাগালি) দিমু না তো কুলে (কোলে) বহাইয়া (বসিয়ে) ক্ষীরমোহন খাওয়ামু?’
চন্দ্র জয়ধর বলল, ‘এই কামটা তুমি ভালা কর নাই বিন্দাবন। অন্যের জমিনে হাবিজাবি ফালাইলে ম্যাজাজ (মেজাজ) কী ঠিক থাকে?’
অন্য বয়স্ক উদ্বাস্তুরা চন্দ্রর কথায় সায় দিল।–-’না না, এইডা ঠিক অয় (হয়) নাই।‘
বৃন্দাবন বলল, ‘আমি ইচ্ছা কইরা ফালাই নাই। পালমশয়ের জমিনের গাছের শিকড় পায়ে বাইজা (লেগে) পইড়া গ্যাছে—’
কিন্তু পাশে দাঁড়াবার মতো কারওকেই পাওয়া গেল না। অন্যের বউকে ভাগিয়ে এনে শেখরনাথের কৃপায় জেফ্রি পয়েন্টে দিব্যি বৃন্দাবনরা কাটিয়ে দিচ্ছে, পনেরো বিঘা সরকারি জমিও পেয়েছে, এটা উদ্বাস্তুরা কেউ মেনে নিতে পারছে না।
গগন বিশ্বাস বলল, ‘হেয়া (তা) যা-ই অউক (হোক), তুমার কিন্তুক হুইশার (হুঁশিয়ার) অইয়া শিকড় বাকড় আগাছার বোঝাহান লইয়া যাওন উচিত আছিল।‘
বৃন্দাবন হতাশ। কেউ তার যুক্তিতে কান দিচ্ছে না। সারা জেফ্রি পয়েন্টের উদ্বাস্তুরা যেন তার বিরুদ্ধে জোট বেঁধেছে। এই শত্ৰুপুরীতে কতজনের সঙ্গে যুদ্ধ করা সম্ভব? গলার স্বর চড়িয়ে সে। যদি বলে তার সঙ্গে যা করা হচ্ছে সেটা আদৌ সুবিচার নয়; বৃন্দাবন জানে মুখ ফসকে এই কথাগুলো বেরিয়ে এলে সবাই মিলে তাকে ছিঁড়ে খাবে। সে দিশেহারা হয়ে পড়ল। এদিকে পায়ের বুড়ো আঙুলটা যন্ত্রণায় টনটন করছে। কী করবে, কী বলবে যখন ভেবে পাচ্ছে না সেইসময় মায়া একেবারে আগুন ধরিয়ে দিল। এতক্ষণ প্রায় নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকেছে। হঠাৎ হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো চেঁচিয়ে উঠল।–এই আপনেগো বিচার অইল (হল)! হেই থনে (থেকে) এট্টা মাইনষেরে (একটা মানুষকে) হুদাহুদি (শুধু শুধু) বাপ-মা তুইলা গাইলাইতে আছে (গালাগালি দিচ্ছে), তার কুনো দুষ (কোনও দোষ) নাই, তভু আপনেরা কেও (কেউ) একহান (একটা) আঙ্গুল তুলবেন না?
মাখনের বউ কালী ফের অগ্নিমূর্তি হয়ে খাই খাই করে উঠল।–’খানকি মাগীর চোপা দ্যাহেন (দেখুন)। তরে (তোকে) না কইছি চুপ মাইরা থাকবি! ফির (আবার) চোপা লাড়তে আছস (নাড়ছিস)? লাইত্থাইয়া (লাথি মেরে) তর (তোর) মুহ (মুখ) ভাইঙ্গা দিমু—’
মায়া আগেই খোলস থেকে বেরিয়ে এসেছিস। সেও মারমূর্তি হয়ে কালীর দিকে ছুটে এল।–’আমি খানকি? তুই খানকি, তর মায়ে খানকি, তর মাইয়া বুইন (বোন), চৈদ্দ গুষ্টি খানকি—’
এরপর তুমুল শোরগোল উঠল। কালী মায়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, চন্দ্র জয়ধররা কোনওরকমে তাকে সামলে রেখে সকালবেলায় একটা রক্তারক্তি কাণ্ড থামিয়ে দিল। তবে দুই যুযুধান পক্ষ থেকেই নোংরা, কদর্য খিস্তি খেউড়ের আদানপ্রদান চলতে লাগল। বুড়ো, আধবুড়ো উদ্বাস্তু যারা মাখন পালের জমিতে জড়ো হয়েছিল তারা সেটা থামাবার চেষ্টা করল না। করলেও ওরা শুনত না।
শুধু কালী বা মায়াই নয়, এখন এই তুমুল কুরুক্ষেত্রে বৃন্দাবন, মাখন এবং মাখনের ছেলেরাও যোগ দিয়েছে। দুনিয়ায় যতরকম বাছা বাছা, কদর্য, অশ্লীল খেউড় তাদের জানা ছিল পরস্পরের দিকে নিক্ষেপ করতে লাগল। পাহাড় সমুদ্র জঙ্গলে ঘেরা নিঝুম জেফ্রি পয়েন্ট এই সকালবেলায় একেবারে সরগরম।
অন্যের ঝগড়াঝাটি বা কোন্দল শোনার মতো আমোদ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কী থাকতে পারে? আরও দূরে দূরে যে উদ্বাস্তুরা তাদের জমিতে কাজ করছিল তারাও শাবল কুড়ুল ফেলে মাখনের জমিতে চলে এল। দগদগে পচা ঘায়ের ওপর ভনভনে মাছির মতো তারা ভনভন করতে লাগল।
মাখন আর বৃন্দাবনদের মহাযুদ্ধ হয়তো সারাদিন ধরেই চলত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হল না।
.
জেফ্রি পয়েন্টের শেষ মাথায় শেখরনাথ আর বিনয় তাদের ঘরে বসে কথা বলছিলেন। অন্য দিন চাটা খেয়েই শেখরনাথরা জমিতে জমিতে ঘুরে উদ্বাস্তুদের কাজকর্ম লক্ষ করেন। কারও কোনও অসুবিধা বা সমস্যা দেখা দিলে তার সুরাহা করে দেন। কিন্তু শেখরনাথের শরীরটা ভোর থেকে ম্যাজম্যাজ করছিল, তাই ঠিক করে রেখেছিলেন একটু বেলার দিকে বেরুবেন। কিন্তু ইহল্লার তীব্র-আওয়াজ জেফ্রি পয়েন্টের বায়ুস্তর ভেদ করে এত দূরে চলে এসেছিল। তাই আর ঘরে বসে থাকা গেল না।
শেখরনাথ বিনয়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ চকিত হয়ে উঠলেন। কান খাড়া করে একটানা সেই শব্দপুঞ্জ শুনতে লাগলেন। বিনয়ও তা শুনতে পেয়েছিল। সে জিগ্যেস করল, ‘কী ব্যাপার কাকা? এত চেঁচামেচি হচ্ছে কেন?’
শেখরনাথের কপালে ভাঁজ পড়েছে। বললেন, ‘নিশ্চয়ই কোনও ফ্যাসাদ বেধেছে। চল তো দেখি—’
শেখরনাথের পরনে ঘরোয়া পোশাক। লুঙ্গি আর হাফশার্ট। বিনয়ের পরনে আধময়লা পাজামা আর হাফ-হাতা গেঞ্জি। সেই অবস্থাতেই পায়ে চটি গলিয়ে দু’জনে বেরিয়ে পড়লেন। ওদিকে পুনর্বাসন দপ্তরের বেশ কয়েকটি কর্মী আর পরিতোষ বণিককেও দেখা গেল। তারা হন্তদন্ত উত্তরের জমিগুলোর দিকে চলেছে।
শেখরনাথের চোখে পড়ল, উত্তরে পেরিমিটার রোডের কাছাকাছি অনেক মানুষের জটলা। আন্দাজ করে নিলেন ওখানেই কিছু একটা ঘটেছে। বললেন, ‘তাড়াতাড়ি চল বিনয়। ব্যাপার সুবিধের মনে হচ্ছে না।’
দুজনে জোরে জোরে পা চালিয়ে দিলেন এবং কয়েক মিনিটের ভেতর মাখন পালের জমিতে পৌঁছে গেলেন।
শেখরনাথদের এবং পুনর্বাসনের কর্মী আর পরিতোষকে দেখে ভিড়টা সরে সরে পথ করে দিল। রণরঙ্গিণী মায়া আর কালী চুপ করে গেছে। একদিকে বৃন্দাবন, অন্যদিকে মাখন আর তার ছেলেদের মুখেও কুলুপ। সমস্ত আবহাওয়াটাই একেবারে স্তব্ধ। একটু আগেও যে এখানে মহাযুদ্ধ চলছিল এখন তা বোঝার উপায় নেই।
ওদিকে পুনর্বাসনের আমিন বর্মী লা-ডিন আর একজন কর্মচারী দৌড়ে গিয়ে দু’টো চেয়ার নিয়ে এল। শেখরনাথ বসতে বসতে বললেন, ‘কী হয়েছে? এত হইচই কেন?’
মাখন তার জমির কোণের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল, ‘ওই দ্যাহেন (দেখুন) বড়কত্তা, বিন্দাবন নিজের জমিনের শিকড়বাকড়, বনতুলসী আইনা আমার জমিনে ফালাইছে।‘ তার মুখ, ভাবভঙ্গি নিপাট ভালমানুষের মতো, ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না এমন একটা মিনমিনে চেহারা। সে জানে শেখরনাথ এমন একজন মানুষ যার কাছে কোনও জারিজুরি, শয়তানি খাটবে না।
তার কথা শেষ হওয়ার আগেই বৃন্দাবন চেঁচিয়ে উঠল।–’মিছা কথা কাকা। এই মাখা সাক্ষাইত (সাক্ষাৎ) শয়তান।‘
সঙ্গে সঙ্গে তুলকালাম বেধে গেল। মাখনরা দলে ভারী, বৃন্দাবনরা মাত্র দু’জন। সবাই পরিত্রাহি চিৎকার করতে করতে একে অন্যের দিকে আঙুল তুলে যা বলে যাচ্ছে তার কিছুটা বোঝা যায়, বাকিটা দুর্বোধ্য। দু’পক্ষই গলা এত চড়িয়েছে যে কানের পর্দা ফেটে যাবার দাখিল।
শেখরনাথের প্রবল ব্যক্তিত্ব থাকলেও তিনি কখনও উঁচু গলায় কথা বলেন না। সবসময় শান্ত, সামান্য গম্ভীর। কিন্তু এই মুহূর্তে সহনশক্তিতে যেন চিড় ধরল। ক্ষিপ্র পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। হাত তুলে কঠোর স্বরে বললেন, ‘একদম চুপ। আমি যাকে বলতে বলব সে-ই শুধু বলবে।’–বৃন্দাবন তুমি আগে বল।
কিভাবে আগাছা এবং শিকড়বাকড়ের বিশাল বোঝা মাথায় চাপিয়ে মাখন পালের জমির ওপর দিয়ে পুবদিকের পাহাড়ের নিচে সেগুলো ফেলে আসতে যাবার সময় একটা গাছের শিকড়ে পা আটকে পড়ে যাওয়ায় মাথার বোঝাটা ছিটকে পড়ে বাঁধন ছিঁড়ে গিয়ে সব ছত্রখান হয়ে পড়ে তার। সবিস্তার বিবরণ দিয়ে যায় বৃন্দাবন। তারপর পা’টা সামান্য তুলে বলে, ‘এই দ্যাহেন (দেখুন) আমার বুইড়া (বুড়ো) আঙ্গুলহান ফাইটা রক্তারক্তি অইছে। আর মান্না আর অর (ওর) গুষ্টি কয় আমি নিকি (নাকি) ইচ্ছা কইরা হের (তার) জমিনে আগাছা উগাছা ফালাইছি। আপনেই বিচার করেন বড়কত্তা–’ একটু দম নিয়ে ফের শুরু করে, ‘য্যাতই হেরে (তাকে) বুঝাই ইচ্ছা কইরা করি নাই। হ্যায় (সে) আর হের (তার) বউ আমারে কী আকথা কুকথা যে কইছে হোনলে (শুনলে) আপনে কানে আঙ্গুল দিবেন। আমারে অরা (ওরা) মাইরাই ফালাইত। মায়া আমারে বাঁচাইতে আইলে মান্নার বউ হেরে (তাকে) কয় কিনা খানকি মাগী। সাচা কথা কই কাকা, মায়াও চেইতা গিয়া (রেগে গিয়ে) হেরেও (তাকেও) খানকি কইছে। কতক্ষণ আর মুহ (মুখ) বুইজা সওন (সহ্য করা) যায়?’
তাকে থামিয়ে দিয়ে শেখরনাথ মাখনের দিকে তাকালেন।–’তোমার কী বলার আছে, এবার বল—’
মাখন বলল, ‘বিন্দাবন মিছা কইছে কাকা। ও ইচ্ছা কইরাই আমার জমিনে শিকড়বাকড় ফালাইছে—’
লোকটার চোখমুখ এবং বলার ভঙ্গি লক্ষ করে বোঝা যাচ্ছে সে সত্যি বলছে না। শেখরনাথ জিগ্যেস করলেন, ‘বৃন্দাবন তো আজই তার জমির শিকড় আর বনতুলসী কেটে তোমার জমির ওপর দিয়ে পুবদিকের পাহাড়ে ফেলতে যায় নি, আমি তাকে বেশ কয়েকদিন যেতে দেখেছি। কই, আগে তো কখনও এখানে ফেলে নি। আজ তার এমন দুর্মতি হবে কেন? তা ছাড়া ইচ্ছা করেই কি নিজের পায়ে রক্তারক্তি কান্ড বাধিয়েছে?’
মাখন বারকয়েক ঢোক গিলল। জবাব দিল না।
শেখরনাথ এবার জনতাকে লক্ষ করে বললেন, ‘তোমরা তো এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিলে। কে ঠিক বলছে আর কে বেঠিক বলছে, তোমরাই বল—’
একজন আধবুড়ো উদ্বাস্তু, নাম অধর ঢালী, বলল, ‘আমরা নিজের চৌখে দেহি (দেখি) নাই। তয় (তবে) বিন্দাবনগো লগে মাখনগো কাইজা (ঝগড়া) বাধার পর দৌড়াইয়া আইছি—’
ভিড়ের অন্য সবাই তার কথায় সায় দিল।
শেখরনাথ তাদের বললেন, তোমাদের কী মনে হয়, বৃন্দাবনের পায়ের বুড়ো আঙুল যে ফেটে গেল সেটা কি সে ইচ্ছা করে ফাটিয়েছে?
সবাই চুপ।
বৃন্দাবন এবার ভয়ে ভয়ে বলল, কাকা, ‘আমার একহান (একটা) কথা আছে।’
শেখরনাথের চোখ বৃন্দাবনের দিকে ফিরল।–’কী কথা?’
‘আপনে সনাতনরে এই কুলোনি (কলোনি) থিকা মইদ্য আন্ধারমানে (মধ্য আন্দামানে) পাঠাইয়া দেওনের (দেবার) পর এইহানকার (এখানকার) অন্য রিফুজরা আমার আর মায়ার লগে কথা কয় না। দূর থিকা আমাগো হুনাইয়া হুনাইয়া (শুনিয়ে শুনিয়ে) কত কু কথা যে কয়! আপনেরে অ্যাদ্দিন কই নাই। (বলি নি)। আমারে কয় কুচরিত্তির, ঢ্যামনা, পরের বউরে ভাগাইয়া আনছি। মায়ারে কয় বেবুইশ্যা (বেশ্যা)। ইট্ট (একটু) ছুতানাতা পাইলে আমাগো ছিড়া খাইব। হেই লেইগা (সেজন্য) চুপ কইরা থাকি। আইজ মাথা থিকা (থেকে) আগাছার বুঝাহান (বোঝাটা) পইড়া যাইতে এই ছুতাহান (ছুতোটা) পাইয়া মাখন পালেরা গুষ্টিসুদ্ধা আমাগো দুইজনরে গাইল (গালাগালি) তত দিছেই (দিয়েছেই), আপনেরা না আইয়া (এসে) পড়লে আমাগো শ্যাষ (শেষ) কইরা ফালাইত (ফেলত)। এই হগল (সব) কথা অ্যাতদিন আপনেরে কই নাই। আইজ না কইয়া পারলাম না। এইর (এর) এট্টা বিহিত করেন কাকা–’ সে হাতজোড় করে কাকুতি মিনতি করতে লাগল।
সমস্ত ব্যাপারটা শেখরনাথের কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে। তিনি মাখন এবং অন্যান্য উদ্বাস্তুদের উদ্দেশে বললেন, ‘আমি বৃন্দাবনদের এখানে থাকতে দিয়েছি। তোমরা ওর পেছনে যদি লাগো তার ফল খুব খারাপ হবে। মাখন, তোমার এত সাহস হয় কী করে? আর একবার যদি শুনি বৃন্দাবনদের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়েছ, এখানে থাকতে পারবে না। জমিজমা কেড়ে নিয়ে লরিতে তুলে তোমাদের পোর্টব্লেয়ারে নিয়ে ছেড়ে দেব। কলকাতায় যে ফিরে যাবে, তার উপায় নেই। জাহাজের টিকিট কেটে দেওয়া হবে না। নিজেদের পেটের ভাত তোমাদেরই জোগাড় করে নিতে হবে। সরকারি কোনওরকম সাহায্য তোমরা পাবে না। সেটা তোমাদের পক্ষে ভাল হবে কিনা, ভেবে দেখ—
ভয়ে মাখনের মুখ সাদা হয়ে গিয়েছিল। ত্রস্ত ভঙ্গিতে সে বলল, ‘কাকা, আমাগো দুষ (দোষ) অইয়া (হয়ে) গ্যাছে। কামটা (কাজটা) ভালা করি নাই। এমুন (এমনটা) আর কুনোদিন অইব (কোনওদিন হবে না। মাফ কইরা দ্যান—’
স্থির, কঠিন দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ মাখনের দিকে তাকিয়ে রইলেন শেখরনাথ। তারপর বললেন, ‘আমার কথাগুলো মনে থাকে যেন। চারপাশের ভিড়টাকে লক্ষ করে বললেন, ‘বৃন্দাবন আর মায়ার সঙ্গে অসভ্যতা, ইতরামি করলে তোমরাও কেউ পার পাবে না।’
এরপর পরিতোষ বণিকের দিকে তাকালেন শেখরনাথ।–’বৃন্দাবনের পাটা জখম হয়েছে; এখনও রক্ত পড়ছে। এখানে ফার্স্ট এডের জিনিসপত্র আছে না?’
পরিতোষ ঘাড় কাত করল।–’আছে কাকা–’
‘এক্ষুনি কারওকে দিয়ে ফাস্ট-এড বক্সটা এনে ওষুধপত্র লাগিয়ে বৃন্দাবনের পায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে। দেবার ব্যবস্থা কর।‘
পরিতোষ চোখের ইশারায় পুনর্বাসনের একজন কর্মীকে ওষুধপত্র আনতে পাঠিয়ে দিল। শেখরনাথের সব দিকে নজর। বৃন্দাবনকে বললেন, ‘তোমার মাথা থেকে মাখনের জমিতে যে জঞ্জাল পড়ে গেছে; সেগুলো আগে সাফ করে পুব দিকের পাহাড়ে ফেলে আসবে। তারপর নিজেদের জমির কাজ ফের শুরু করবে।
‘হেইডা (সেটাই) ভাইবা (ভেবে) রাখছিলাম (রেখেছিলাম)। পালমশয় হের (তার) আগেই আমাগো চৈদ্দ (চোদ্দ) গুষ্টির—’
বৃন্দাবনকে থামিয়ে দিয়ে শেখরনাথ বললেন, ‘যা হবার হয়ে গেছে। ওসব ভুলে যাও। তোমাকে। আর জেফ্রি পয়েন্টের সব উদ্বাস্তুকে বলছি, ফের যেন কোনওরকম অশান্তি না হয়। দেশভাগের পর সব হারিয়ে এদেশে এসেছ। আন্দামান দ্বীপে পা রাখার জায়গা পেয়েছ। সবাই একসঙ্গে মিলেমিশে থাকো। ঘরবাড়ি তোল, জমি চৌরস করে চাষবাস কর। তা নয়, সামান্য কারণে ঝগড়া! কূটকচালি! আমার কথাগুলো মনে থাকে যেন।’
শেখরনাথ আর বসলেন না। শরীরটা ভাল নেই। তার ওপর হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়ায় বেশ অসুস্থই লাগছে। বিনয়কে সঙ্গে নিয়ে তিনি নিজেদের ঘরের দিকে পা বাড়ালেন।
.
৪.১৬
কোনও কোনওদিন রাতের খাওয়াদাওয়া চুকিয়ে নিজেদের ঘরে এসে নানা বিষয়ে কথা বলতে বলতে শেখরনাথ অবধারিত যে প্রসঙ্গে চলে আসেন তা হল স্বাধীনতা। বিনয় আগেই জেনে গেছে, স্বাধীনতার নামে এই খণ্ডছিন্ন দেশকে তিনি মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেন নি। দু’শো বছরের পরাধীনতা থেকে এই যে মুক্তি, সেটা কি আদৌ মুক্তি! সারা দেশে না হলেও বাঙালির জীবনে যে দগদগে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে তা কি কোনওদিন নিরাময় হবে?
আজ টেবিলের ওপর দু’টো তেজী হ্যারিকেন জ্বলছিল। জেফ্রি পয়েন্ট গভীর ঘুমে তলিয়ে আছে। সমস্ত চরাচর একেবারে নিঝুম। খোলা জানলার বাইরে কুয়াশায় ঢাকা পাহাড় এবং জঙ্গল ঝাপসা ঝাপসা। সমুদ্রটা চোখেই পড়ে না। কিন্তু পাহাড়প্রমাণ উঁচু উঁচু ঢেউগুলোর অবিরল পাড়ে আছড়ে পড়ার শব্দ ভেসে আসছে। মাঝে মাঝে রাতজাগা পাখির কর্কশ চিৎকার এবং ঝিঁঝিদের একটানা গলাসাধা ছাড়া বিশ্বব্রহ্মান্ডের কোথাও আর কোনও আওয়াজ নেই। প্রতিটি রাতেই জেফ্রি পয়েন্টের চেহারা ঠিক এইরকম হয়ে যায়।
বিনয় তার বিছানায় বসে ছিল, শেখরনাথ একটু দূরে তার বিছানায় বালিশে হাতের ভর রেখে আধ-শোওয়া মতো হয়ে কথা বলছিলেন, ‘জানো বিনয়, পাকিস্তান হওয়ার পর জিন্না বলেছিলেন, ‘আমরা একটা ‘মথ-ইটন’ অর্থাৎ পোকায়-কাটা মুসলিম জাহান পেলাম। ভারতবর্ষ কি তার চেয়ে ভাল কিছু পেয়েছে? ক্ষতে-ভরা, রক্তাক্ত, বিধ্বস্ত এক দেশ।’
শেখরনাথ যা ভুলতে পারেন না, যা সারাক্ষণ তাঁকে ভেতরে ভেতরে তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় বিদ্ধ করে সেটাই আজ আবার বলতে লাগলেন, ‘এই স্বাধীনতার সবচেয়ে ওয়স্ট সাফারার আমরা– বাঙালিরা। পাঞ্জাবেরও প্রচুর রক্ত ঝরেছে। হাজার হাজার মানুষ সেখানেও খুন হয়েছে, অগুনতি তরুণী ধর্ষিত হয়েছে, গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছে। তবে ওদের মোটামুটি একটা স্বস্তিও মিলেছে। টোটাল এক্সচেঞ্জ অফ পপুলেশন। এপারের মুসলমানরা পশ্চিম পাঞ্জাবে চলে গেছে, ওপারের হিন্দু আর শিখেরা ইস্ট পাঞ্জাবে চলে এসেছে। যদিও তা বাঞ্ছিত ছিল না। অখণ্ড, স্বাধীন ভারতের কনসেপ্টের সঙ্গে তা একেবারেই মেলে না। কিন্তু এটা মন্দের ভালো। তাছাড়া সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট সিন্দুক খুলে পাঞ্জাবের রিহাবিলিটেশনে টাকার বস্তা ঢেলে দিয়েছে। কত রকমের যে দান-খয়রাত। এদিকে বাঙালি উদ্বাস্তুদের জন্য সরকারের হাতের মুঠি খুলতেই চায় না।’
বিনয় এসব জানে। তবু নীরবে শুনতে থাকে।
শেখরনাথ থামেন নি।–’একেক সময় আমার কী মনে হয় জানো? বেঙ্গলেও এক্সচেঞ্জ অফ পপুলেশন হলে বোধহয় ভাল হত।’
বিনয় বেশ অবাকই হল।–’আপনি এরকম ভাবছেন কেন কাকা?’
‘পাকিস্তান রাষ্ট্রটার জন্মই হয়েছে শত্রুতা, বিদ্বেষ, ঘৃণা আর অবিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে। দু’বছরেরও বেশি হল পাকিস্তান তো কায়েম হয়ে গেছে। পূর্ব বাংলায় যে হিন্দু, বৌদ্ধ আর খ্রিস্টানরা ছিল তারা তো নতুন দেশটাকে স্বদেশ বলে মেনেও নিয়েছিল। তবু সেখানে বার বার একতরফা দাঙ্গা হচ্ছে কেন? কেন মাইনোরিটির নিরাপত্তা নেই? চোদ্দ পুরুষের ভিটেমাটি খুইয়ে কেন স্রোতের মতো উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবাংলা, আসাম আর ত্রিপুরায় পালিয়ে আসছে?’
বিনয় শেখরনাথের দিকে তাকিয়ে থাকে; উত্তর দেয় না।
শেখরনাথ কারণটাও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দিলেন, ‘আসলে একটা কট্টর ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রে মাইনোরিটিরা থাকতে একেবারেই ভরসা পাচ্ছে না। লিবারেল ইসলামিক স্টেট হলে এই সমস্যা হত না। ধর্মান্ধতা যে কী সাংঘাতিক সমস্যা সৃষ্টি করে, ভাবতে সাহস হয় না। ভারত আর পাকিস্তান এমন দুই রাষ্ট্র যে একটা দেশে কিছু ঘটলে তার প্রতিক্রিয়া এসে পড়ে আরেকটা দেশে। ইন্ডিয়ায়, বিশেষ করে পশ্চিমবাংলায় তার কিছু কিছু লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আন্দামানে বসে তো মেনল্যাণ্ডের সমস্ত খবর পাই না। তবে শুনেছি, ওয়েস্ট বেঙ্গলে দু-চার জায়গায় মাইনোরিটি কমিউনিটির লোকজনের ওপর হামলা হয়েছে। দেশভাগের পর দুই দেশে শান্তি আসবে এটাই কাম্য ছিল কিন্তু বাস্তবে কী দেখা যাচ্ছে? ইংরেজরা কি চিরকাল মারামারি কাটাকাটির জন্যে এই সাব-কন্টিনেন্টকে দু’টুকরো করে দিয়ে গেল? যা চলছে তাতে মনে হয় পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানরা থাকতে পারবে না। এটা আমরা চাইনি। পূর্ব পাকিস্তানে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লিবারেল বাঙালি অনেকেই আছেন। কিন্তু তারা আর ক’জন! বেশির ভাগই উন্মাদ হয়ে গেছে।’
মধ্যরাতে জেফ্রি পয়েন্টের এই ঘরটার পরিবেশ হঠাৎ থমথমে হয়ে যায়।
অনেকক্ষণ নিজের মধ্যে মগ্ন হয়ে রইলেন শেখরনাথ। দূরমনস্কর মতো কী ভাবছেন, বোঝা যাচ্ছেক না। বিনয় নিঃশব্দে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল।
একসময় শেখরনাথ হঠাৎ বলে উঠলেন, ‘দেশভাগের জন্যে শুধুমাত্র ইংরেজদের দোষারোপ করা ঠিক নয়। মূল চক্রী যদিও তারাই তবু আমাদের নেতারাও দায় এড়াতে পারেন না। স্বাধীনতার আগে সেই সময়কার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী একবার ঘোষণা করেছিলেন, উনিশ শো আটচল্লিশের মাঝামাঝি কোনও একটা সময় ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে এবং ইংরেজরা দু’শো বছরের এই কলোনি ছেড়ে চলে যাবে। অস্বীকার করা যাবে না, গান্ধিজিও চেয়েছেন দেশটা দুটুকরো না করে কংগ্রেস কিছু দাবি মেনে নিয়ে মুসলিম লিগের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসুক। তিক্ততা, অবিশ্বাস কাটিয়ে দেশ শাসনের ভার তারা একসঙ্গে নিক। তুমি কি এসব জানো?’
বিনয় জানত না; আস্তে মাথা নাড়ল। উদ্বাস্তুদের প্রসঙ্গে এটলি, গান্ধিজি, কংগ্রেস আর মুসলিম লিগকে হঠাৎ কেন নিয়ে এলেন শেখরনাথ, বোঝা যাচ্ছে না। কোন গহন পথে তার চিন্তার ক্রিয়া চলছে, কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না।
শেখরনাথ বলতে লাগলেন, তুমি একজন সাংবাদিক। উদ্বাস্তু হয়ে ইণ্ডিয়ায় চলে এসেছ। দেশের, বিশেষ করে দেশভাগের ইতিহাসটা তোমার জানা দরকার। তাঁর বলার ভঙ্গিতে ভর্ৎসনার সুর। ‘কলকাতায় ফিরে গিয়ে ইতিহাসটা ভাল করে পড়ে নিও। নইলে পার্টিশানের পারসপেক্টিভটা ঠিকমতো ধরতে পারবে না।’
বিনয় সংকোচে কুঁকড়ে গিয়েছিল। শেখরনাথ ঠিকই বলছেন, ইতিহাসটা তার বিশেষভাবে জানা প্রয়োজন।
শেখরনাথ থামেন নি।কিন্তু জিন্না ছিলেন নাছোড়বান্দা। অ্যাটলি বা গান্ধিজির প্রস্তাব তিনি কোনওমতেই মেনে নেবেন না। মাউন্টব্যাটেনেরও এটা পছন্দ হয় নি। জিন্না একটা সেপারেট দেশের জন্যে তখন মরিয়া। হী ওয়ান্টস এ সেপারেট মুসলিম নেশন–পাকিস্তান। নেহরু, প্যাটেল এবং কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতারাও এটলির প্রস্তাব মেনে নেন নি। নেহরুরা যে কোনও শর্তে স্বাধীনতা চাইছিলেন। আসলে বয়েস হয়ে যাচ্ছিল। হাতের নাগালে ওখত্ তাউস। সিংহাসনে চড়ার লোভ কখনও ছাড়তে পারে? ক্ষমতারূপী সুপক্ক আম্রফলটি নাকের ডগায় ঝুলছে। নেহরু প্যাটেলদের মনের অবস্থাটা বুঝতেই পারছ। ভাবখানা সারাজীবন অনেক কষ্টটষ্ট করেছি, প্রচুর জেল টেল খেটেছি, সুযোগ যখন এসে গেছে ক্ষমতাটা ভোগ তো করে নিই।
‘গান্ধিজি ক্ষোভে, দুঃখে দিল্লি ছেড়ে বিহারে, বিহার থেকে কলকাতার বেলেঘাটায় গিয়ে বসলেন। মাউন্টব্যাটেন ঠিক এটাই চাইছিলেন। গান্ধিজি এই সময় দিল্লিতে থাকুন, সেটা তার অভিপ্রেত ছিল না। স্পষ্ট জানি না, তবে একটা কথা আমার মনে হয়—’
উৎসুক সুরে বিনয় জিগ্যেস করে, ‘কী কথা কাকা?’
শেখরনাথ বললেন, ‘নেহরু প্যাটেলরাও হয়তো তাই চাইছিলেন। গান্ধিজি দিল্লিতে থাকলে দেশভাগটা তিনি আটকাতে পারতেন কিনা বলতে পারব না; মাউন্টব্যাটেন, নেহরু বা জিন্নাদের পক্ষে খুবই অস্বস্তির কারণ হত। একটা কথা ভেবে আমার ভীষণ ধন্দ লাগে—’
বিনয় প্রশ্ন করল না। শেখরনাথের দিকে পলকহীন তাকিয়ে রইল।
শেখরনাথ বলেই চলেছেন, ‘গান্ধিজি কতবার অনশনে বসে কত অসাধ্যসাধন করেছেন কিন্তু দেশভাগের মতো একটা নিদারুণ সিদ্ধান্ত সাত তাড়াতাড়ি নিতে যাওয়া হচ্ছে, তার কী মারাত্মক ফলাফল হতে পারে, সেটা একবার ভেবে দেখলেন না! কোটি কোটি মানুষের ভাগ্য কয়েক লহমায় স্থির হতে চলেছে, অথচ গান্ধিজি অনশনে বসার কথা তো এই চরম মুহূর্তে নিতে পারতেন। বলতে তো পারতেন, দেশ ভেঙে টুকরো করার সিদ্ধান্ত আমি মানি না। আমৃত্যু অনশনে বসছি। নেহরু প্যাটেল জিন্না বা মাউন্টব্যাটেন যতই সর্বশক্তিমান হোন না, গান্ধিজি অনশনে বসলে দেশ ভাঙার শর্তে স্বাধীনতা অত সহজ হত না। গান্ধিজি কতবার বলেছেন, স্বাধীনতা এলে কংগ্রেসকে ভেঙে দেওয়া উচিত। দেশভাগ যখন হয় হয় সেই সময় কংগ্রেসকে ডিসব্যান্ড করার কথা একবার যদি মুখ ফুটে উচ্চারণ করতেন, নেহরুদের হাজারবার পার্টিশনের কথা ভাবতে হত। তিনি তা করলেন না। বরং রাজনীতির মূল সেন্টার দিল্লি থেকে বারো চোদ্দ শো মাইল দূরে কলকাতায় গিয়ে মুখ বুজে মৌনী হয়ে বসে থাকলেন! এত বড় মর্মান্তিক ঘটনা ঘটতে চলেছে সব জেনে বুঝেও তিনি একটি আঙুল পর্যন্ত তুললেন না। কী বলব তাকে? এসকেপিস্ট? পলাতক? বুঝতে পারছি না।
‘ছেচল্লিশের ষোলই আগস্ট জিন্নার ডাকে সারা ভারত জুড়ে যে নিদারুণ দাঙ্গা শুরু হয়েছিল তাতে প্রায় দশ লক্ষ মানুষ খুন হয়েছে, দেশের দুই প্রান্তে দেড় কোটিরও বেশি মানুষ তাদের চোদ্দপুরুষের বাড়িঘর থেকে উৎখাত হয়েছে। কয়েক লক্ষ তরুণীকে ধর্ষণ এবং অপহরণ করা হয়েছে। বড়লাটের কাছের সাঙ্গোপাঙ্গরা এটাকে তেমন গুরুত্ব দিতেই রাজি হয় নি। নিস্পৃহ মুখে বলেছে, এতবড় একটা দেশ স্বাধীনতা পেতে চলেছে, তার জন্যে এই মূল্যটুকু খুব বেশি নয়। ভাবা যায়? বড়লাট কি এটা জানতেন না? নিশ্চয়ই জানতেন। তবে তার মন্তব্য জানা যায় নি।
‘বেলেঘাটা থেকে সারা দেশের ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়ে বসে থাকা ছাড়া গান্ধিজির হয়তো আর কিছুই করার ছিল না। খালিকুজ্জামান বলেছিলেন, ভারতের ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে অন্ধকার সময়। জাতির জনক গান্ধিজিকে আমি কিন্তু এসকেপিস্ট বলতে রাজি নই। এই মহান মানুষটিকে শুধু বলতে পারি ভারতীয় ইতিহাসের খুব সম্ভব সবচেয়ে ট্রাজিক চরিত্র। এটা আমার মত।’
আবার কিছুক্ষণের জন্য ঘরের ভেতর নৈঃশব্দ্য নেমে এল। শুধু অদূরে সেই সমুদ্রগর্জন আর ঝিঁঝিদের কনসার্ট চলছেই। বিরামহীন। রাতজাগা পাখিগুলোর সাড়াশব্দ নেই। খুব সম্ভব তারা এতক্ষণ ডাকাডাকির পর ঘুমিয়ে পড়েছে।
একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শেখরনাথ বললেন, ‘জিন্না সেইসময় কঠিন অসুখে ভুগছিলেন। সেটা ইনকিউরেবল ডিজিস। রোগটা মুসলিম লিগের কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় নেতা হয়তো জানতেন। হয়তো বা জানতেন না। সুচতুরভাবে এই রোগের কথা গোপন রাখা হয়েছিল। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলি যে উনিশ শো আটচল্লিশের মাঝামাঝি ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন, ততদিন অপেক্ষা করলে দেশভাগ হয়তো এড়ানো যেত। কারণ জিন্না বেশিদিন বাঁচেন নি। মৃত্যুর আগে পাকিস্তান কায়েম করার জন্যে তাই অদম্য জেদ ধরেছিলেন। হয়তো অনুমান করেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর মুসলিম লিগের পক্ষে পাকিস্তান আদায় করার মতো তাঁর মাপের বিশাল, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অন্য কোনও নেতা নেই। মৃত্যুর আগে যা করার তাঁকেই করতে হবে। পাকিস্তান তার চাইই চাই। এদিকে কংগ্রেস নেতৃত্বেরও তর সইছিল না। স্থির হয়ে গেল দেশটা ভাগ করেই স্বাধীনতা আসবে। ভারত ভাগ্যবিধাতারও খুব সম্ভব সেই ইচ্ছাই ছিল।’
একটানা বলার পর থামলেন শেখরনাথ। বিনয় অবাক হয়ে ভাবে, সেই কবে বিশের দশকে যাবজ্জীবন কালাপানির দন্ডাদেশ নিয়ে আন্দামানে সাজা খাটতে এসেছিলেন শেখরনাথ। তারপর একদিনের জন্যও ইন্ডিয়ার মেনল্যান্ডে ফিরে যাননি। অথচ দেশের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন বঙ্গোপসাগরের এই সুদূর দ্বীপপুঞ্জে থেকেও দেশের সমস্ত ইতিহাস তার জানা। মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে থাকে বিনয়।
শেখরনাথ ফের শুরু করলেন, ‘যাই হোক, মাত্র কয়েক বছর আগে কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজের ডাক দিয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে শুরুর দিকে তা পাওয়া যায়নি। ডমিনিয়ন স্টেটাস নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। কিছুদিন পরেই অবশ্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতা এসেছে। এদিকে দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে শাসনভার ভাগ করে দেবার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেল পুরোদমে। পনেরোই আগস্ট দেশ স্বাধীন হবে। তার মধ্যে দেশটাকে তো ভাগ-বাঁটোয়ারা করার কাজটা শেষ করা দরকার। তাই জুলাই মাসে স্যার সিরিল র্যাডক্লিফকে লন্ডন থেকে ভারতে উড়িয়ে আনা হল। তার কর্মক্ষমতা সম্পর্ক বড়লাট মাউন্টব্যাটেনের বিরাট আস্থা। কিন্তু ভারত সম্পর্কে পুঁথিগত কিছু ধারণা তার থাকতে পারে, তবে বাস্তব জ্ঞানবুদ্ধি কতটুকু সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এই লোকটিকেই পাঞ্জাব আর বাংলা ভাগ করে ভারত এবং পাকিস্তানের সীমানা ঠিক করে দেবার দায়িত্ব দেওয়া হল। তিনি হলেন পূর্ব এবং পশ্চিম দু’দিকের বাউন্ডারি কমিশনের চেয়ারম্যান। হাতে দু’মাস কয়েকদিন মাত্র সময়; এর মধ্যে বাংলা আর পাঞ্জাবের কোন কোন ডিস্ট্রিক্ট বা ডিস্ট্রিক্টের কতটা অংশ ভারত আর পাকিস্তান পাবে তা ঠিক করে দিতে হবে। এত বড় একটা দেশ ভাগ হবে, সেজন্য সময় মাত্র দু’মাস। স্বাধীনতার জন্যে এমন একটা অর্বাচীন খামখেয়ালি সিদ্ধান্তও মেনে নিতে হয়েছিল। আশ্চর্য, লিগ বা কংগ্রেসের নেতারা মুখ বুজে তা মেনে নিয়েছিলেন, কেউ সামান্য আপত্তি পর্যন্ত করেন নি। এমন একটা ভবিতব্যের কথা কে ভাবতে পেরেছিল?’
একটু থেমে শেখরনাথ আবার শুরু করলেন, ‘র্যাড ক্লিফ মাউন্টব্যাটেনের পরম আস্থাভাজন। আমি যতদূর জানি এই ধুরন্ধর ইংরেজটি আগে আর কখনও ভারতে আসেননি। নতুন দায়িত্ব পেয়ে টেবিলে ইন্ডিয়ার ম্যাপ বিছিয়ে তিনি ছুরি কাঁচি পেন্সিল নিয়ে বসলেন। দেশটা কাটাছেঁড়া হবে কিসের ভিত্তিতে? বেসিসটা কী? শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক ভাগাভাগিটাই সাব্যস্ত হল। এই নিয়ে অশান্তি, উত্তেজনা কম হয়নি। বেঙ্গল আর পাঞ্জাবের কোন কোন ডিস্ট্রিক্ট, ডিস্ট্রিক্টের অংশ, ভারত বা পাকিস্তানে পড়বে তাই নিয়ে মানচিত্রে ছুরির দাগ পড়তে লাগল। নেতারা, বিশেষ করে পাঞ্জাবের বড় বড় নেতারা যখন রে রে করে উঠলেন, নতুন মানচিত্র এনে আবার নতুন করে সীমানা ঠিক করা হল। বার বার এই সীমানা বদলানো হতে লাগল। যশোর খুলনা পশ্চিমবঙ্গে আসা উচিত ছিল। সিলেট ডিস্ট্রিক্ট আসামের সঙ্গে থাকাই সঙ্গত ছিল কিন্তু বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কায় আসামের নেতারা কোনও ভাবেই তাতে রাজি হলেন না। সামান্য কয়েক দিনে কোটি কোটি মানুষের ভাগ্য স্থির করে ফেললেন র্যাডক্লিফ। আমি তো বলব, ভারতের ইতিহাসে এটা আরও একটা অন্ধকার সময়।’
ইতিহাসের এই জটিল দিকগুলো ততটা জানা ছিল না বিনয়ের। সে অবাক হয়ে শুনে যাচ্ছে। দেশভাগ যে এই প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধা প্রাচীন বিপ্লবীটির হৃদয়ে কতটা ক্ষত সৃষ্টি করেছে, টের পাওয়া যাচ্ছে। কী উত্তর দেবে, ভেবে পেল না বিনয়।
ইতিহাসের সেই মর্মান্তিক ভয়াবহ সময় আজ যেন প্রবলভাবে শেখরনাথের ওপর ভর করেছে। তিনি ভেতরকার চাপা যন্ত্রণা ক্রমাগত উগরে দিতে লাগলেন।–’পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর জিন্না কী ভরসা দিয়েছিলেন? পাকিস্তানের যারা নাগরিক হবে তার ধর্ম যাই হোক, হিন্দু, খ্রিস্টান বৌদ্ধ, শিখ–সবাই নিরাপদে, সসম্মানে থাকতে পারবে। তাদের স্বাধীন ধর্মাচরণে, সামাজিক অনুষ্ঠানে কোনও রকম বাধার সৃষ্টি বরদাস্ত করা হবে না। রাষ্ট্র তার সবরকম নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। প্রশাসনের চোখে হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান বা শিখের মধ্যে এতটুকু ভেদাভেদ, বৈষম্য করা হবে না। পাকিস্তানের প্রতিটি মানুষ হবে সেই দেশের সম্মানিত নাগরিক। জিন্নার হয়তো এই রকমই সদিচ্ছা ছিল। কিন্তু বাস্তবে কী দেখা গেল?’
বিনয় মগ্ন হয়ে শুনে যাচ্ছিল। নিজের অজান্তেই তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল—’কী?’
‘পাকিস্তানে মাইনোরিটি কমিউনিটি বিশেষ করে হিন্দু আর শিখরা কি নিরাপদে থাকতে পারল? জিন্না দীর্ঘজীবী হন নি; পাকিস্তান হাসিল করার কিছুদিনের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়। বেঁচে থাকতে থাকতেই তিনি দেখে গেছেন পাকিস্তানে যে ভয়ঙ্কর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল তাতে লাখে লাখে হিন্দু এবং শিখ দুই সীমান্ত দিয়ে ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। আমার কী মনে হয় জানো?’
‘কী?’
‘জিন্না পাকিস্তান চেয়েছিলেন এবং তাঁর দাবি মতো একটা দেশ আদায়ও করে ছেড়েছিলেন–এসব ঠিক। কিন্তু তিনি কট্টরপন্থী বা গোঁড়া সাম্প্রদায়িক ছিলেন বলে মনে হয় না। কিন্তু মৃত্যুর আগে এমন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন যে ফান্ডামেন্টালিস্টদের নিয়ন্ত্রণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্রশাসনের লাগামও তার শীর্ণ শিথিল মুঠি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। তার ফল হয়েছিল এই, লক্ষ লক্ষ মানুষকে সীমান্তের ওপার থেকে এপারে বাস্তুহারা হয়ে চলে আসতে হল। হল কী? এখনও পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু আসার বিরাম নেই। আমার কী মনে হয় জানো?’
উত্তর না দিয়ে বা প্রশ্ন না করে উন্মুখ তাকিয়ে রইল বিনয়।
শেখরনাথ থামেন নি।–’পাকিস্তানে মাইনোরিটি যতকাল আছে এই উদ্বাস্তু স্রোত কখনও থামবে না।
এরপর অনেকক্ষণ নীরবতা।
হঠাৎ একসময় শেখরনাথ একেবারে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন।–’তুমি কি যুগান্তর, অনুশীলন সমিতি, ব্ৰতী সমিতি, স্বদেশ বান্ধব সমিতি, সুহৃদ ও সাধনা সমিতি–এই নামগুলো শুনেছ?’
বিনয় অবাক।–’যুগান্তর আর অনুশীলন সমিতি ছাড়া আর কোনও নাম শুনিনি।‘
‘মাত্র কয়েকটার নাম বললাম। আন-ডিভাইডেড বেঙ্গলে এরকম অজস্র গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠেছিল। সবই সশস্ত্র বিপ্লবীদের সংগঠন। অবশ্য পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, ইউ পি এবং আরও কয়েকটা প্রভিন্সেও এমন অনেক সমিতিও অ্যাক্টিভ ছিল। বিপ্লবীরা মনে করত, লক্ষ বছর চরকা কাটলেও কিচ্ছু হবে না। মিনমিনে, ভ্যাদভেদে অহিংস আন্দোলনে দেশের স্বাধীনতা আসবে না। ওসব আকাশকুসুম কল্পনা। ইংরেজদের ঝাড়ে মূলে তাড়াতে হলে বন্দুক পিস্তল ছাড়া উপায় নেই।
‘সারা দেশের কথা থাক। বাংলার কথাই বলি। সবচেয়ে বেশি গুপ্ত সমিতি ছিল বাংলাতেই। হাজার হাজার তাজা তরুণ ইংরেজদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার তুলে নিয়ে লড়াই করেছে। ধরা পড়ে জেলখানায় পচে মরেছে, কত প্রাণ যে ফাঁসির দড়িতে শেষ হয়ে গেছে তার সীমাসংখ্যা নেই। এই মৃত্যুঞ্জয়ী শহিদদের ক’জনকে আমরা মনে রেখেছি?’
এই বিপ্লবীদের কথা আগেও কয়েকবার বলেছেন শেখরনাথ। নিঝুম মধ্যরাতে দেশভাগের কথা বলতে বলতে ফের সেই প্রসঙ্গ কেন তুললেন, বিনয় বুঝতে পারছে না। সে অপেক্ষা করতে লাগল।
নিজের ঝোঁকে বলে যেতে লাগলেন শেখরনাথ।–’পাঞ্জাব, ইউ পি, মহারাষ্ট্র–সারা দেশের বিপ্লবীরা স্বাধীনতার জন্যে অনেক স্যক্রিফাইস করেছে। এঁদের সবাইকে প্রণাম জানিয়েও বলব, পাঞ্জাবি আর বাঙালিদের স্যাক্রিফাইসের তুলনা নেই। তার নীট ফলটা কী দাঁড়াল? দুটো প্রভিন্সই দুটুকরো হয়ে গেল। লক্ষ লক্ষ মানুষ জন্মভূমি খেয়াল। লক্ষ লক্ষ মানুষ খুন হল, তাদের ঘরের যুবতী মেয়েদের লুট করে ধর্ষণ করে হত্যা করা হল। বিপ্লবীদের আত্মদানের বিনিময়ে বাঙালি আর পাঞ্জাবিদের কি এটাই প্রাপ্য ছিল বিনয়? দুটো প্রভিন্স এত মূল্য দিল আর স্বাধীনতা নামে ইংরেজরা যা দিয়ে গেল তার সুফলটা ভোগ করছে বাকি ভারত। একটা ব্যাপার লক্ষ কর, বিপ্লবীদের ত্যাগের, আত্মদানের ইতিহাসটাকে আর গুরুত্বই দেওয়া হচ্ছে না। আমার ভয় হয়–’ বলে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। শেখরনাথ। তারপর শুরু করলেন, আক্ষেপে ক্ষোভে হতাশায় তাঁর কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে এল।-–’বিরাট নিঃশব্দ একটা চক্রান্ত চলছে।‘
সবিস্ময়ে বিনয় জিগ্যেস করে, ‘কিসের চক্রান্ত কাকা?’
‘ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লবীদের অবদানের ইতিহাস সম্পূর্ণ মুছে যাবে। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, বাঘা যতীন থেকে উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত, সাভারকর ব্রাদার্স থেকে সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তীদের তো মাথায় করে রাখা উচিত ছিল। সেই মর্যাদা কি তাদের দেওয়া হচ্ছে? স্বাধীন ভারত ওঁদের ভুলে যাবে, নীরবে অস্বীকার করবে, কোনওদিন কি ভাবা গিয়েছিল?’
প্রাক্তন বিপ্লবীর বেদনার্ত কণ্ঠস্বর আন্দামানের দূর প্রান্তে জেফ্রি পয়েন্টের একটি ঘর থেকে বাইরে ছড়িয়ে পড়ল। নিঝুম রাতে চারিদিকের পাহাড়ে জঙ্গলে তার প্রতিধ্বনি হতে লাগল।
.
৪.১৭
একদিন রাত্রে সুভাষচন্দ্রের কথা উঠল।
সারাদিন উদ্বাস্তুদের নিয়ে ব্যস্ত থাকেন শেখরনাথ। তাদের কাজকর্মের তদারক করেন। যদি কারও কোনও সমস্যা দেখা দেয় তার সুরাহা করে দেন। পুনর্বাসন দপ্তর এবং বনবিভাগের অজস্র কর্মী রয়েছেন। তবু শেখরনাথের মনে হয়, দেশ থেকে উৎখাত হয়ে আসা এই মানুষগুলোর সমস্ত দায়িত্ব তারই। অপার মায়ায় তিনি যেন তার শেষ জীবনের সঙ্গে এই মানুষগুলোকে জড়িয়ে নিয়েছেন।
কিন্তু রাত্রিবেলা জেফ্রি পয়েন্ট যখন নিশুতিপুর সেই সময় দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়কদের আত্মত্যাগের নানা কাহিনি শোনান শেখরনাথ। আজ বললেন, ‘দেশভাগের কথা উঠলেই সুভাষচন্দ্রকে আমার বিশেষ করে মনে পড়ে।’
বিনয় রীতিমতো অবাক হল।–-‘এ আপনি কী বলছেন কাকা! পার্টিশনের সময় নেতাজি তো দেশেই ছিলেন না। এমন একটা প্রচার করা হয়েছে যে পার্টিশনের অনেক আগেই প্লেন ক্র্যাশে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।’
শেখরনাথ বললেন, ‘নেতাজির এই মৃত্যুর রটনাটা বড়ই রহস্য। দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের বিশ্বাস প্লেন ক্রাশে তাঁর মৃত্যু হয় নি। এই মৃত্যুর প্রসঙ্গ থাক। আমার আশা একদিন না একদিন এই রহস্য ভেদ করে আসল সত্যটা বেরিয়ে আসবে।’
বিনয় চুপ করে রইল।
শেখরনাথ বলতে থাকেন, ‘দেশের জন্যে সুভাষচন্দ্রের অবদানের কথা একবার ভাবো। আই সি এস হওয়ার পর পরম আরামে তিনি বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু নিজস্ব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আরাম কেরিয়ারের কথা ভাবেন নি সুভাষ। অবশ্য স্বীকার করতেই হবে গান্ধিজি, জওহরলাল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, জে এম সেনগুপ্ত থেকে রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সর্দায়, প্যাটেল এমন বিরাট বিরাট জননায়করা কেউ ক্ষুদ্র স্বার্থের কথা ভাবেন নি। দেশই ছিল তাঁদের কাছে টপ প্রায়োরিটি। দেশের স্বাধীনতার জন্যে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। দেশের কোটি কোটি মানুষকে তারা উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। গান্ধিজির কথা নতমস্তকে মানতেই হবে। তাঁর মত এবং পথের সঙ্গে আমাদের মতো সশস্ত্র বিপ্লবীদের মতাদর্শের মিল নেই। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে এসে ডান্ডি অভিযান, অসহযোগ আন্দোলন, আইন-অমান্য আন্দোলন, কুইট ইন্ডিয়া আন্দোলনের ডাক দিয়ে তিনি দেশ জুড়ে যে জনজাগরণ ঘটিয়েছিলেন কে তা অস্বীকার করবে? তিনিই বোধহয় প্রথম দেশনেতা যাঁর ডাকে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। গান্ধিজির কথা মাথায় রেখেও বলব নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এ দেশে একজন বিরল জননেতা।’
জিজ্ঞাসু ছাত্রের মতো বিনয় প্রশ্ন করে, ‘কোন দিক থেকে বলছেন?’
‘দেখ, কংগ্রেসের নেতারা প্রায় সবাই ছিলেন আপসকামী। আলাপ-আলোচনা করে, অহিংস আন্দোলন চালিয়ে তারা ইংরেজদের কাছ থেকে স্বাধীনতা ভিক্ষে করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইম্পিরিয়েলিস্টরা কে কবে ভ্যাদভেদে গালগল্প করে বুঝদার সুবোধ বালকের মতো কলোনি ছেড়ে দেয়? বিশেষ করে ইন্ডিয়ার মতো একটা এতবড় কলোনি, যেখানে কত মধু! এ দেশের ওয়েলথ লুট করে ব্রিটিশ এম্পায়ার ফুলে ফেঁপে উঠেছে। মুখের কথায় সেই বিশাল মৌচাক কেউ ছাড়ে! এসব আকাশ কুসুম কল্পনা। স্বপ্ন আর বাস্তবের মধ্যে অনেক ফারাক। গান্ধিজি অহিংস নীতিতে বিশ্বাস করতেন। অহিংসাই ছিল তার ধর্ম। আমি সেটা সম্মান করি। কিন্তু তার ডাকা কোনও কোনও আন্দোলন সহিংস, হিংস্র আকার ধারণ করলে তিনি তার রাশ টেনে ধরেছেন। ফলে স্বাধীনতা কবে পাওয়া যাবে সে সম্বন্ধে সংশয় দেখা দিয়েছে। দেশের মুক্তি, আমার মনে হয়, এর ফলে ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছিল।
‘কিন্তু কাকা—’ পুরোটা বলা হল না, দ্বিধান্বিতভাবে থেমে গেল বিনয়।
‘বলো বলো, চুপ করে গেলে কেন?’
‘সুভাষচন্দ্রও তো একসময় কংগ্রেসে ছিলেন।’
‘কী বলতে চাও, বুঝতে পেরেছি। সুভাষ অবশ্যই কংগ্রেসে ছিলেন, গান্ধিজিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। সবই ঠিক। কিন্তু কংগ্রেস নামে প্রতিষ্ঠানটিতে কি তাঁর পক্ষে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকা সম্ভব হয়েছে? আগেই বলেছি কংগ্রেসের আপসকামী নীতির সঙ্গে তাঁর মতের মিল হচ্ছিল না। স্বাধীনতার প্রশ্নে তিনি আন-কমপ্রোমাইজিং। এর ফলে তাকে কংগ্রেসের ভেতর থেকেই চরম বিরোধিতার মুখে পড়তে হয়েছে। পর পর দু’বছর উনিশ শো আটত্রিশ এবং উনচল্লিশে নানা বিরোধিতার মধ্যেও সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন, এতটাই ছিল তাঁর জনপ্রিয়তা। কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টকে সেই আমলে রাষ্ট্রপতি বলা হত। প্রথমবার তিনি রাষ্ট্রপতি হলেন হরিপুরায়, দ্বিতীয়বার ত্রিপুরীতে। হরিপুরায় সভাপতি হওয়ার পর একটা বছর কোনওরকমে কাটিয়ে দিতে পারলেও ত্রিপুরী কংগ্রেসে ফের জয়ী হয়ে যখন ফের রাষ্ট্রপতি হলেন তখন সংঘাতটা চরমে উঠল। স্বয়ং গান্ধিজি চাইছিলেন, আবার সুভাষচন্দ্র রাষ্ট্রপতি হোন। ত্রিপুরীতে তাঁর মনোনীত প্রার্থী ছিলেন পট্টভি সীতারামাইয়া। সুভাষচন্দ্র নির্বাচিত হলে গান্ধিজি স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, ‘সিতারামাইয়াস ডিফিট ইজ মাই ডিফিট।’ নিজের ব্যক্তিগত পরাজয় বলেই সুভাষচন্দ্রের জয়কে ধরে নিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র যাতে সুশৃঙ্খলভাবে কাজ না করতে পারেন সেজন্যে তার ইঙ্গিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বাররা সুভাষচন্দ্রের প্রতি অনাস্থা তো প্রকাশ করলেনই, পদত্যাগও করে বসলেন। একজন নির্বাচিত সভাপতির সঙ্গে এমন আচরণ নিঃসন্দেহে খুবই বেদনাদায়ক। কংগ্রেস যে মাত্র একটি মানুষের নির্দেশে চলবে সেটা আগেই স্থির হয়েছিল। তার মনঃপূত নয়, এমন কিছু ঘটলে যাঁর যত সমর্থনই থাক, তাকে তিনি মেনে নেবেন না। হতাশ, মর্মাহত সুভাষচন্দ্রের পক্ষে এত বড় একটা রাজনৈতিক দল চালানো অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। এমন অসহযোগিতা প্রত্যাশা করেননি সুভাষচন্দ্র। কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তিনি বেরিয়ে এলেন এবং নতুন দল ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠা করলেন।
‘সুভাষচন্দ্রের চরিত্রে স্বাধীনতার প্রশ্নে আপসকামিতার স্থান ছিল না। এই শব্দটা মনেপ্রাণে অপছন্দ করতেন। কংগ্রেসি রাজনীতির মধ্যে কতরকম যে জটিলতা, কত অদৃশ্য দড়ি টানাটানি, তা মর্মে মর্মে তিনি অনুভব করেছেন।
‘নতুন দল তৈরি করলেন ঠিকই কিন্তু বুঝতে পারছিলেন ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে থেকে তিনি ব্রিটিশ রাজত্বের বিরুদ্ধে যে ধরনের সংগ্রাম চান সেটা মোটেই সম্ভব নয়। এই সংগ্রামে তিনি সেভাবে সমর্থন পাবেন না, বিশেষ করে সব চেয়ে বড় রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের কাছ থেকে তো বটেই। মুসলিম লিগের অন্য উদ্দেশ্য রয়েছে; তাদের পাশে পাওয়ার কল্পনা নেহাতই দুরাশা। দেশের বিপ্লবী দলগুলোর তখন ছন্নছাড়া, ভাঙাচোরা হাল। একটা দলের সঙ্গে অন্য দলের সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত। তাছাড়া এই সব দলের অজস্র ছেলে তখন জেলে পচছে, হাজার হাজার বিপ্লবীকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে মারা হয়েছে। বাকি যারা আছে তারা মানসিক দিক থেকে বিপর্যস্ত।
‘ছোটখাটো আরও বহু পলিটিক্যাল পার্টি তখনও ছিল কিন্তু তাদের মতাদর্শ অন্যরকম। এদের সমর্থন সম্বন্ধে সুভাষ হয়তো সন্দিহান ছিলেন। দেশের ভেতরে থেকে দেশের স্বাধীনতা লাভ সম্পূর্ণ দুরূহ। যা কিছু করতে হবে দেশের বাইরে গিয়ে।’
বিনয় জিগ্যেস করল, ‘সুভাষচন্দ্র কি এসব কোথাও লিখে গেছেন?’
শেখরনাথ বললেন, ‘আমার চোখে তা পড়ে নি। বহু বছর মেনল্যাণ্ড থেকে অনেকদূরে এই আন্দামান দ্বীপে পড়ে আছি। কলকাতা থেকে ক’টা বইই বা এখানে আসে!’
‘তা হলে আপনার এরকম ধারণা হল কিভাবে?’
‘সুভাষচন্দ্রের জীবন, রাজনৈতিক চেতনা, তার স্বাধীনতা লাভের পদ্ধতি, সেই সময়ের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, অন্য পলিটিক্যাল পার্টিগুলোর এজেণ্ডা– এসব লক্ষ করলে তেমনটাই মনে হয়। তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিলেন ব্যাপকভাবে অস্ত্র হাতে তুলে না নিলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে সোনার খনিরূপ ভারতবর্ষের কলোনি থেকে দূর করা যাবে না। তাই—’ বলে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন শেখরনাথ।
খুব মগ্ন হয়ে শুনছিল বিনয়। বলল, ‘তাই কী?’
আনমনা ভাবটা কেটে গেল শেখরনাথের। বিনয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘ছদ্মবেশে গোয়েন্দাদের সতর্ক চোখে ধুলো ছিটিয়ে কাবুল হয়ে কয়েকটা দেশ ঘুরে চলে গেলেন জার্মানি; সেখান থেকে সাবমেরিনে জাপান। পুরোদমে তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। জাপানি ফৌজ দুরন্ত গতিতে ভারতের দিকে ধেয়ে আসছে। প্রচারের ভাষায় ব্রিটিশবাহিনী ‘সাকসেসফুল রিট্রিট’ অর্থাৎ সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করছে। সুভাষচন্দ্র এই সুযোগটা নিলেন। গড়ে তুললেন প্রবাসী ভারতীদের, হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিস্টান সবাইকে নিয়ে এক দুর্বার বাহিনী। এদের অনেকে মিত্রপক্ষের সেনাবাহিনীতে ছিল। বাকিদের মিলিটারি ট্রেনিং দিয়ে নেওয়া হয়। গড়ে উঠল আজাদ হিন্দ ফৌজ ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি। মেয়েরাও এগিয়ে এসেছিল; গড়া হল মরণজয়ী নারী বাহিনী। আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিটি সেনানীর হৃদয়ে সুভাষচন্দ্র জ্বালিয়ে দিলেন–স্বাধীনতার মশাল। প্রতিটি সৈনিক তখন একেকটি আগুনের শিখা।
‘একটা ফ্রন্ট ধরে জাপ-বাহিনী, অন্য এক ফ্রন্ট ধরে আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনারা অভিযান শুরু করেছে। বিনয়, তুমি কল্পনা করতে পার, সুভাষচন্দ্র তাঁর অনুগামী সব সৈনিকের জন্যে ‘কমন কিচেন’-এর ব্যবস্থা করেছিলেন। শিখ হিন্দু মুসলিম সবাই পাশাপাশি বসে খেত। ভারতের আর কোনও রাজনৈতিক দল বা জননেতা কি এটা করতে পেরেছিলেন? আমার জানা নেই। তার সেনাদের মর্মে এই বার্তাটি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু পৌঁছে দিয়েছেন, স্বাধীনতার চেয়ে বড় কিছু নেই। ধর্ম নিজস্ব ব্যাপার। আই এন এর প্রতিটি সৈনিক ভাবত প্রথমে তারা ভারতবাসী, তারপর হিন্দু, মুসলিম, শিখ বা খ্রিস্টান। মাতৃভূমির মুক্তি তাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি। দেশের মানুষকে একসূত্রে আর কেউ কি এভাবে গাঁথতে পেরেছেন, পেরেছেন কি তাদের পরস্পরের এত কাছে নিয়ে আসতে? আমার জানা নেই।
‘একদিন সচকিত ভারতবর্ষ শুনতে পেল সেই অবিস্মরণীয় কণ্ঠস্বর, ‘আমি সুভাষ বলছি—’ তারপর দেশবাসীকে আহ্বান জানালেন, এই মুক্তিযুদ্ধে তারাও যেন যুক্ত হয়। গান্ধিজি, জওহরলাল থেকে বড় বড় জননায়কদের তিনি আবেদন জানালেন এই সুবর্ণসুযোগ যেন হাতছাড়া না হয়। ইউরোপে আফ্রিকায় এশিয়ায় চারিদিকে মিত্রশক্তি, বিশেষ করে ইংরেজ বাহিনী বেধড়ক মার খাচ্ছে, জার্মান বোমায় লণ্ডনের সিকি ভাগ ধ্বংস হয়েছে, পৃথিবী-জোড়া সাম্রাজ্যের গরিমা যাদের, তাদের অর্থনীতি চুরমার হতে চলেছে, দু’শো বছরের দম্ভ চুপসে গেছে, এই সময় যদি ভারতের ভেতর তুমুল আন্দোলন শুরু করা যায়, ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট স্বাধীনতা দিতে বাধ্য।
‘সারা দেশ জুড়ে তখন শিহরন। প্রবল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর নেতারা সুভাষচন্দ্রের ডাকে সাড়া তো দিলেনই না, উলটে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানালেন। একদল বলল, সুভাষচন্দ্র ফ্যাসিস্ট শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। তিনি তোজোর কুকুর। কুইসলিং। জাপানিদের ডেকে এনে ফ্যাসিস্টদের হাতে দেশকে তুলে দিতে চান। অথচ সেকেন্ড গ্রেট ওয়ারে ইম্পিরিয়ালিস্ট ব্রিটেনের সঙ্গে রাশিয়া যখন হাত মেলায় তখন সেটাকে পিপলস ওয়ার বলা হয়।
‘সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, একসময় সুভাষচন্দ্র যখন কংগ্রেস ছেড়ে চলে আসেন নি, তিনি এবং জওহরলাল, দু’জনেই ছিলেন যুব ফ্রন্টের নেতা। এঁদের ঘিরেই তরুণ ভারত স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল। দু’জনের মধ্যে ছিল গভীর বন্ধুত্ব।
‘জওহরলাল কোথায় সুভাষচন্দ্র এবং তার আজাদ হিন্দ বাহিনীকে স্বাগত জানাবার জন্যে সারা দেশ জুড়ে আন্দোলনের ডাক দেবেন, তা নয়। সুভাষের ভারত-অভিযানকে কংগ্রেস এবং দেশের অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর মতো একেবারেই পছন্দ করলেন না। অন্য সব জননেতা তো বটেই জওহরলালও তার মতামত স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন। সুভাষ বাহিনী ভারতে প্রবেশ করুক তিনি তা চান না।
‘অ্যালায়েড ফোর্স কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজকে রুখতে পারে নি, দেশের ভেতর বহুদূর পর্যন্ত চলে এসেছিল এই বাহিনী। কোহিমার কাছাকাছি ময়রাঙে এসে জাতীয় পতাকা তুলেছিল। বিনয়, তুমি জাহাজ থেকে নেমে পোর্টব্লেয়ারে এসেই জানতে পেরেছিলে, এবারডিন মার্কেটের কাছে জিমখানা ময়দানেও জাপবাহিনীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্র চলে এসেছিলেন। এখানেও জাতীয় পতাকা তুলেছেন। সেলুলার জেল দেখাতে দেখাতে সেদিন তোমাকে বলেছি সেখানেও সুভাষ এসেছিলেন। তিনি জাতীয় পতাকা তুলে দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষণও দিয়েছেন। যেসব ইংরেজ এখানে ছিল তারা কুকুরের মতো পালিয়ে গিয়েছিল। জাপান সরকার তাদের ফৌজ কিছুদিন এখানে রাখলেও সুভাষচন্দ্রকেই এই দ্বীপপুঞ্জের পূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছিলেন। নিশ্চয়ই ভুলে যাও নি।’
বিনয় আস্তে মাথা নাড়ল–‘না। এই ইতিহাস কি ভোলা যায়?’
‘সুভাষ দু-তিনদিনের বেশি এখানে থাকতে পারেন নি। মণিপুর কোহিমা ফ্রন্টের দিকে তাকে চলে যেতে হয়েছিল। দেশের মাটিতে এই তার শেষ পদার্পণ। বিশাল ব্রিটিশ কলোনির সামান্য একটু অংশকে কিছুদিনের জন্যে অন্তত তিনি স্বাধীন করতে পেরেছিলেন। দেশের তখনও ঘুম ভাঙে নি। কিংবা বলা যায়, দেশনেতারা একরকম নীরবই ছিলেন।
‘জাতির চরম দুর্ভাগ্য, আজাদ হিন্দ ফৌজের পরাজয় ঘটে। তার কারণ রণকৌশলের ত্রুটি বা বাহিনীর উদ্যম এবং দেশপ্রেমের অভাব নয়। জাপান বর্মা অবধি এসেও আর এগুতে পারেনি, মিত্রশক্তি তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এই প্রচণ্ড প্রত্যাঘাত জাপানের পক্ষে সামলানো সম্ভব হয়নি। তাদের রিট্রিট অর্থাৎ পিছু হটতে হয়েছিল। এই অবস্থায় আজাদ হিন্দ ফৌজকে সাহায্য করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। পেছন থেকে অস্ত্রের সাপ্লাই, রি-ইনফোর্সমেন্ট সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। খালি হাতে, খালি পেটে তো যুদ্ধ চালানো যায় না।
‘ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির অসংখ্য সেনানী আর সেনানায়করা অ্যালায়েড ফোর্সের হাতে ধরা পড়লেন। দিল্লির লালকেল্লায় শাহনওয়াজ, ধীলনদের যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিচার শুরু হল। এইবার দেশের টনক নড়ল যেন। সারা ভারতবর্ষ উত্তাল হয়ে উঠল। আজাদ হিন্দের বীর সেনানীদের মুক্তির দাবিতে দিকে দিকে আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। তাদের দমন করার জন্যে ইংরেজের পুলিশ গুলি লাঠি তো চালালই, ব্যাপক ধরপাকড়ও শুরু করল। কিন্তু দেশজোড়া বিপুল জনজাগরণকে ঠেকানোর সাধ্য তাদের ছিল না। প্রতিটি ভারতবাসীর মুখে তখন শুধু ‘নেতাজি সুভাষ’ আর ‘আজাদ হিন্দ ফৌজ’। একটা ইনফরমেশন দিচ্ছি; শুনলে তুমি অবাক হবে বিনয়। এইসময় সারা দেশের নানা প্রান্তে, এমনকি দক্ষিণ ভারতেও যে শিশুরা জন্মেছে তাদের নামকরণ হয়েছিল সুভাষচন্দ্রের নামে। দেশ কোন চোখে, কী অসীম শ্রদ্ধায় তাঁকে দেখত একবার ভেবে দেখ বিনয়।‘
এটা বিনয়ের জানা ছিল না। কারণ সে তখন পুব বাংলার এক কোণে রাজদিয়ার মতো একটা নগণ্য আধা-গ্রাম আধা-শহরে রয়েছে। প্রকাণ্ড দেশের কতটুকু খবরই বা সেখানে পৌঁছত! অনন্ত বিস্ময়ে সে তাকিয়ে থাকে।
শেখরনাথ বলতে থাকেন, ‘দেশ জুড়ে যে স্বতঃস্ফূর্ত উন্মাদনা তাতে বেগতিক হয়ে পড়লেন কংগ্রেস নেতারা। ভুলভাই দেশাই আর জওহরলাল কালো কোট পরে লাল কেল্লায় ধীলন আর শাহনওয়াজদের মুক্তির দাবিতে সওয়াল করতে নেমে পড়লেন। যাঁরা একদিন সুভাষের আজাদ হিন্দ বাহিনীকে রুখবার জন্যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তাঁরা রাতারাতি বদলে গেলেন। ভাবখানা এই, আজাদ হিন্দ এবং সুভাষের সঙ্গে আমরাও আছি। ভাবা যায়?
‘সুভাষচন্দ্রের কর্মকাণ্ডের ইমপ্যাক্ট কতদূর ছড়িয়ে পড়েছিল চিন্তা করা যায় না। করাচি এবং বোম্বাইতে নৌবিদ্রোহ শুরু হয়ে গেল। ইংরেজ তখন ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে। বিদ্রোহ শুধু নেভির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে এমন কোনও কথা নয়। তাদের আতঙ্ক সেটা সেনাবাহিনী এবং এয়ারফোর্সের মধ্যেও যে কোনও মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়তে পারে। কংগ্রেস নেতারা, যতদূর মনে হয় প্যাটেল বুঝিয়ে সুঝিয়ে নৌবাহিনীকে শান্ত করলেন। তুমুল আন্দোলন ধীরে ধীরে থেমে গেল। আর কোর্ট মার্শাল করে নেভির কর্তারা শত শত সোনার টুকরো ভারতীয় তরুণ অফিসারকে হত্যা করল। এই নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য নেই, কেউ একটা আঙুল পর্যন্ত তুলল না।
‘সেই সময়ের ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেট এটলি একটি সার সত্য উচ্চারণ করেছিলেন। একটি ভাষণে তিনি বলেছেন, সুভাষচন্দ্র যুদ্ধে জিততে পারেন নি, তার অভীষ্ট পূর্ণ হয়নি, এসব ঠিক কিন্তু তার সামরিক কর্মকাণ্ড ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। ভারতের স্বাধীনতা একদিন আসত কিন্তু সুভাষের পরাজয় সেটা অনেক এগিয়ে এনেছিল।
‘আসলে ব্রিটিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের শিরদাঁড়া আতঙ্কে কেঁপে গিয়েছিল। আর্মি, নেভি এবং এয়ার ফোর্সে হাজার হাজার ভারতীয় সেনানী এবং অফিসার রয়েছে। সুভাষচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় তারা যদি ব্যাপকভাবে বিদ্রোহ ঘটায়, সেই সঙ্গে আসমুদ্র হিমাচল সাধারণ মানুষেরা তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে, ইংরেজ দশদিনও ভারতের মাটিতে টিকে থাকতে পারবে না। চাটিবাটি গুটিয়ে যে কলোনি তাদের জন্য সোনার ডিম পাড়ে সেটি পেছনে ফেলে জাহাজ কি প্লেনে উঠে চিরকালের মতো পালাতে হবে। দেশবাসীর দুর্ভাগ্য সুভাষচন্দ্রের অভিযান এবং স্বপ্ন সফল হয়নি। যদি হত তবে দেশভাগ করে স্বাধীনতা আসত বলে আমার মনে হয় না। এই সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারা তিনি কিছুতেই মেনে নিতেন না। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস কিভাবে লেখা হত, আমার জানা নেই।
দীর্ঘ সময় অবিরল বলে যাওয়ার পর চুপ করলেন শেখরনাথ। বিনয় কোনও প্রশ্ন করল না। নীরবে প্রাক্তন বিপ্লবীটির দিকে তাকিয়ে রইল।
একসময় গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে শেখরনাথ বললেন, ‘যা সর্বনাশ ঘটার তা তো ঘটেই গেছে। আচ্ছা বিনয়, তুমি কি জানো, নেতাজি সুভাষচন্দ্র একটি ভাষণে কী বলেছিলেন?’
কোন ভাষণটির কথা শেখরনাথ বললেন, সে বিনয় বুঝতে পারছিল না। সে নীরবে তাকিয়ে থাকে।
শেখরনাথ তাকে লক্ষ করেন নি। আপন মনেই বলতে লাগলেন, ‘দেশ স্বাধীন হলে কিভাবে সেটা গড়ে তোলা হবে তার একটা রূপরেখা অনেক আগেই তিনি ভেবে রেখেছিলেন। স্বাধীন ভারতের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, জাতীয় ঐক্য, অর্থনীতিকে নতুন করে গড়ে তোলা। তিনি চেয়েছিলেন প্রতিটি দেশবাসীর জন্য সামাজিক ন্যায়, চেয়েছিলেন সাম্প্রদায়িকতা, জাতিভেদ এবং অস্পৃশ্যতা-মুক্ত পরিবেশ। চেয়েছিলেন দেশের ঐশ্বর্য শুধু হাতে-গোনা কয়েকজনের হাতে না চলে যায়, তার ভাগ যেন সমানভাবে এদেশের মানুষ পায়। সমাজতন্ত্রের কথাও তাঁর মাথায় ছিল। তবে সেই সমাজতন্ত্র মার্ক্সের বই থেকে উঠে আসা কমিউনিজম নয়; রাশিয়ার অন্ধ অনুকরণও নয়। এই দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি,সমাজব্যবস্থা থেকেই তা উঠে আসবে। তার একটা স্বপ্ন সফল হয়নি। তাঁর দ্বিতীয় স্বপ্নটা সার্থক হবে কিনা, ভবিষ্যতেই তা বলতে পারবে।’ একটু থেমে বললেন, ‘অনেক রাত হয়ে গেল; এবার শুয়ে পড়।’
আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়েছে দু’জনে। বাইরে রাত ঝিম ঝিম করছে। বিনয় কিন্তু ঘুমোত পারল না। পাশের বিছানায় শুয়ে থাকা সর্বত্যাগী বিপ্লবীটির অন্তর্লীন দুঃখ, বেদনা, ক্ষোভ, স্বপ্নভঙ্গের আক্ষেপ তার বুকের ভেতরটা খানিক দূরের সমুদ্রের মতো অবিরাম আলোড়নে উথালপাতাল হয়ে যেতে লাগল।
.
৪.১৮
জেফ্রি পয়েন্টের দিনগুলো বাঁধা রুটিনে কেটে যাচ্ছে। একটা দিন যেন আরেকটা দিনের হুবহু কার্বন কপি। সকালে ঘুম ভাঙার পর এখানে কর্মকাণ্ড শুরু হয়ে যায়। উদ্বাস্তুরা সমুদ্রের ধারে ম্যানগ্রোভের ঝোঁপের আড়ালে প্রাকৃত কর্মটি সেরে, মুখটুখ ধুয়ে চা আর বাসি রুটি গুড় খেয়ে যে যার জমিতে চলে যায়। বনতুলসীর উদ্দাম ঝোঁপ, আগাছার ঝাড় বা ছোট ছোট গাছগুলো কাটা, মাটির তলায় অন্য যেসব বুনো গাছের শিকড়বাকড় ছড়িয়ে আছে সেগুলো উপড়ে ফেলা। দুপুরে সূর্য মাথার ওপর উঠে এলে এবেলার মতো কাজ শেষ। ক্লান্ত ছিন্নমূল মানুষগুলো তখন ফিরে এসে সমুদ্রে চান টান সেরে খাওয়াদাওয়া চুকিয়ে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নেয়। তারপর আবার জমিতে গিয়ে ঝোঁপঝাড় সাফাই সেই সূর্যাস্ত অবধি। এর কোনও হেরফের নেই।
চিরকাল পুনর্বাসন দপ্তরের ব্যারাকে থেকে সরকারি লঙ্গরখানায় চারবেলা খেয়ে ইহজীবন কাটিয়ে দেওয়া চলবে না। জমি দেওয়া হয়েছে, সেগুলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চৌরস করে চাষের উপযোগী করতে হবে। শুধু তাই নয়, নিজের নিজের জমির একধারে প্রতিটি পরিবারকে বাড়িও তুলে নিতে হবে। রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্ট এই বাবদে সবরকম সহায়তা দেবে। কিন্তু অনন্তকাল তো এমনটা চলতে পারে না। মূল কথাটা হল উদ্বাস্তুদের স্বয়ম্ভর হতে হবে। ফসল ফলিয়ে, ঘরবাড়ি বানিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে নিজেদের জন্মভূমি থেকে বহুদূরের এই দ্বীপে নিজেদের পায়ে তাদের দাঁড়াতে হবে। পরনির্ভর নয়, স্বাধীন স্বাবলম্বী মানুষ হিসেবে। সরকারের তরফ থেকে সেটাই তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই নির্দেশমতোই উদ্বাস্তুরা দিনভর খেটে চলেছে। পরিশ্রমে তাদের লেশমাত্র গাফিলতি নেই। তারাও স্বাবলম্বী হতে চায়।
কিন্তু বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপপুঞ্জে যেখানে চারিদিকে সমুদ্র, পাহাড়, হাজার বছরের অরণ্য সেখানে সমস্ত কিছুই তো মসৃণ নয়। হিংস্র জারোয়ারা আছে, সমুদ্রে হাঙর আছে, তা ছাড়া উদ্বাস্তুদের নিজেদের মধ্যেও ঝগড়াঝাঁটি কোন্দল আছে। নানারকম সমস্যা। তবু তারই মধ্যে সূর্য-ওঠে, সূর্যাস্ত হয়। প্রাকৃতিক নিয়মে একটা দিনের পর আরেকটা দিন আসে। এই নিয়মের হেরফের নেই।
শেখরনাথ এবং বিনয়ের দৈনিক নির্ঘন্ট প্রায় একইরকম। সকালে উঠে চাটা খেয়ে উদ্বাস্তুদের জমির পর জমিতে ঘুরে বেড়ানো। যাতে নিজেদের মধ্যে ছিন্নমূল মানুষগুলো কোনওরকম হুজ্জত না বাধায় সেদিকে সতর্ক নজর শেখরনাথের। তিনি চান যত দ্রুত সম্ভব পূর্ববাংলার সর্বস্ব হারানো মানুষগুলোর জন্য এই উপনিবেশ গড়ে উঠুক। নির্বিঘ্নে, সুষ্ঠুভাবে। যদি কোনও সংকট দেখা দেয় তিনি তাদের পাশেই থাকবেন। বিনয়ের ভূমিকা পুরোপুরি দর্শকের। বা পর্যবেক্ষকের। সারাদিনে সে যা দেখে, যেসব অভিজ্ঞতা হয়, রাত্রে ‘নতুন ভারত’-এর জন্য সেই সব মালমশলা দিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করে। তারপর শেখরনাথের সঙ্গে দেশের অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক রাত অবধি নানা আলোচনা। বহুজনের হিতে যে বিপ্লবীটি তার শেষজীবনটি সঁপে দিয়েছেন তাঁর কাছ থেকে কত কিছু শোনা যায়, কত কিছু শেখা যায়। এই মানুষটি প্রতিদিন একটু একটু করে বিনয়ের চিন্তাভাবনাকে সমৃদ্ধ করে তুলছেন।
.
শেখরনাথের প্রবল অনিচ্ছা এবং আপত্তি সত্ত্বেও জেফ্রি পয়েন্টের উত্তর দিকের জঙ্গল ফেলিং চলছেই। অরণ্য নির্মূল করে উদ্বাস্তু উপনিবেশের জন্য প্রচুর জমি চাই।
জঙ্গল যত কাটা হচ্ছে, কাল্পনিক পেরিমিটার রোডও ততই পিছিয়ে যাচ্ছে। বুশ পুলিশের উঁচু উঁচু টঙগুলোও খুলে নিয়ে যতদূর পর্যন্ত জমি উদ্ধার হচ্ছে তার প্রান্তে নিয়ে বসানো হচ্ছে। আরও যত জমি উদ্ধার হবে সেইমতো টঙগুলোও সরিয়ে নেওয়া হবে।
একদিন সকালবেলায়, তখনও জেফ্রি পয়েন্টের ব্যস্ততা শুরু হয় নি, কমন কিচেনে চা তৈরির আয়োজন চলছে, শেখরনাথ আর বিনয় তাদের ঘরে বসে কথা বলছিল।
শেখরনাথ বললেন, ‘আমার ভীষণ দুশ্চিন্তা হচ্ছে বিনয়!’
বিনয় অবাক হল।–’কিসের দুশ্চিন্তা কাকা?’
‘যেভাবে উত্তর দিকে বেপরোয়া জঙ্গল কাটা হচ্ছে তাতে জারোয়াদের মধ্যে প্রচণ্ড রি-অ্যাকশন হবে। আমি বহুকাল আন্দামানে আছি। ওখানকার ট্রাইবালদের, বিশেষ করে জারোয়াদের মতিগতি ঠিক বুঝতে পারি। আগেও উদ্বাস্তুদের ওপর বারকয়েক হামলা হয়েছিল। তাতে মোহনবাঁশি তো মরতে বসেছিল। আমার ধারণা, এবার খুব বড় রকমের অ্যাটাক ওরা করবে।‘
বিনয় কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল তার আগেই বুশ পুলিশের দু’জন তাগড়াই চেহারার সিপাই এসে হাজির। তাদের চোখেমুখে আতঙ্ক এবং দুর্ভাবনার ছাপ। শেখরনাথ এদের চেনেন। ওরা হল মাসুদ জান আর জগপত সিং।
দরজার সামনে তারা দাঁড়িয়ে ছিল। হাতের ইশারায় দু’জনকে ঘরের ভেতর ডেকে দুটো বেতের চেয়ার দেখিয়ে বললেন, ‘বোসো। হঠাৎ নজরদারি ছেড়ে টঙের মাথা থেকে চলে এলে যে! কিছু গোলমাল হয়েছে?
বুশ পুলিশরা পালা করে দিনরাত পেরিমিটার রোড বরাবর টঙগুলোর ওপর বন্দুক আর ক্যানেস্তারা নিয়ে জারোয়াদের ওপর নজরদারি চালায়। একেকটা দলের আট ঘন্টা করে ডিউটি। এইভাবে তিন শিফটে তিনটে দল জারোয়াদের গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখে। যদি আন্দামানের এই হিংস্র, আদিম বাসিন্দাদের জেফ্রি পয়েন্টের উদ্বাস্তু কলোনির দিকে আসতে দেখে তক্ষুনি ক্যানেস্তারা পিটিয়ে তুমুল শোরগোল তোলে। তাতে ঘাবড়ে গিয়ে জারোয়ারা আর উদ্বাস্তুদের জন্য নির্দিষ্ট এলাকায় আসে না; উত্তর দিকের গভীর অরণ্যে পালিয়ে যায়। কখনও যদি আসার চেষ্টা করে আকাশের দিকে বন্দুক উঁচিয়ে বার বার ফাঁকা আওয়াজ করে। বন্দুক যে মারাত্মক বিপজ্জনক বস্তু তা অরণ্যবাসী জারোয়ারাও জানে। তারা তখন চিৎকার করতে করতে পালিয়ে যায়। ভারত সরকারের কঠোর নির্দেশ আছে–বুশ পুলিশ ফাঁকা আওয়াজ করতে পারে কিন্তু কোনওভাবেই যেন জারোয়াদের তাক করে গুলি না চালায়। জনজাতি সংরক্ষণের নীতি নেওয়া হয়েছে সরকারি স্তরে। শুধু আন্দামানের জারোয়া, ওঙ্গে আর সেন্টিনালিজদেরই নয়, দেশের যেখানে যত উপজাতি আছে তাদের নিজস্ব পরিবেশে সবরকম নিরাপত্তা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এসব বিনয়ের অজানা নয়।
মাসুদ জান বলল, ‘চাচাজি বহোৎ বুরা খবর—’
‘কিসের খারাপ খবর?’
মাসুদ জান জানায়, জারোয়ারা ক’দিন ধরে পেরিমিটার রোডের কাছাকাছি যখন তখন চলে আসছে। দু-চারজন নয়। শ’য়ে শ’য়ে। মাসুদদের মনে হচ্ছে যে কোনও সময় তারা রিফিউজি কলোনিতে হানা দেবে।
শেখরনাথের কপালে ভাঁজ পড়ল। বললেন, ‘মহা বিপদ।‘
‘আমাদের কী করা দরকার চাচাজি?’
‘হুঁশিয়ার থাকো। আর ওদের দেখলেই জোরে জোরে ক্যানেস্তারা বাজাবে, হল্লা করবে, তেমন বুঝলে ব্ল্যাঙ্ক ফায়ারও করবে। দেখো ওদের গায়ে গুলি টুলি না লাগে—’
জগপত সিং বলল, ‘ইয়াদ আছে চাচাজি। লেকিন ইয়ে জারুয়ালোগ বহোৎ খতরনাক। ওদের জঙ্গল খতম করে রিফুজরা গাঁও বসাতে আসছে, এটা ওরা মানতে চাইছে না। জোর গু হুয়া উনলোগনকা। ওদের সামলানো বহোৎ বহোৎ মুশিবত।‘
আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন শেখরনাথ। চিন্তাগ্রস্তের মতো বললেন, ‘ঠিকই বলেছ। কিন্তু যেভাবে হোক সামলাতে হবেই। ডিউটি ছেড়ে অনেকক্ষণ এসেছ। তাড়াতাড়ি চলে যাও। ভেবে দেখি কী করা যায়—’
কিছুক্ষণ নীরবতা।
তারপর শেখরনাথ থমথমে মুখে বললেন, ‘বিনয়, আমি ঠিক এই ভয়টাই করেছিলাম। বিশুকে, চিফ কমিশনারকে এত করে বোঝালাম, জেফ্রি পয়েন্টের উত্তর দিকে যেটুকু জঙ্গল কাটা হয়েছে সেই পর্যন্তই থাক। বিশু অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের বড় অফিসার হলেও তার কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা নেই। চিফ কমিশনারই আন্দামান নিকোবর আইল্যাণ্ডের সর্বেসর্বা। কিন্তু তিনি কিছুতেই শুনলেন না। উত্তর দিকের জঙ্গল কাটা আগে থেকেই নাকি স্থির হয়ে আছে। জঙ্গল রিক্রম না করলে ইস্ট পাকিস্তানের ডিসপ্লেসড পীপলের পুনর্বাসন হবে কী করে? সংকট দু’দিকের। জঙ্গল কাটলে জারোয়ারা খেপে উঠছে। না কাটলে পুনর্বাসন ধাক্কা খাবে। খবর পেয়েছি দু’মাস পর কলকাতা থেকে আরও দু’শো ফ্যামিলি আসছে।
বিনয় বলল, ‘হ্যাঁ। এটা বিরাট সমস্যা।
‘ভেবে দেখ, এর আগে জারোয়ারা হানা দিয়ে মোহনবাঁশিকে প্রায় শেষই করে ফেলছিল। নেহাত তার আয়ু ছিল, আর সময়মতো তাকে আমরা পোর্টব্লেয়ার হাসপাতালে নিয়ে যেতে পেরেছিলাম, ডাক্তার চট্টরাজ আর টিম ওকে বাঁচিয়ে তুলেছে। মোহনবাঁশি তিরে জখম হওয়ায় এখানকার উদ্বাস্তুরা ভয় পেয়ে তুমুল গোলমাল শুরু করে দেয়। কিছুতেই তারা আন্দামানে থাকবে না। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাদের সামলানো গেছে। মাসুদরা যা বলে গেল, তাতে ভীষণ দুশ্চিন্তা হচ্ছে। প্রথম দিকে দু-চারজন জারোয়া হানা দিয়েছে, কিন্তু এখন শয়ে শয়ে জারোয়াকে পেরিমিটার রোডের কাছাকাছি দেখা গেছে। এতগুলো জারোয়া যদি একসঙ্গে তির টির চালায় কত রিফিউজি যে মার্ডার কি ইনজিওরড হবে, ভাবতে সাহস হয় না।
বিনয় চিন্তাগ্রস্তের মতো তাকিয়ে থাকে। জারোয়াদের সমস্যাটা কিভাবে সামলানো যাবে, সে সম্বন্ধে তার কোনও ধারণাই নেই।
শেখরনাথ বলতে লাগলেন, ‘মোহনবাঁশিকে যখন তির মারা হয় তোমাকে অনুরোধ করে বিশু আর আমি বলেছিলাম, খবরটা যেন তোমাদের পেপারে না বেরোয়। তুমি বুঝতে পেরেছিলে নিউজটা বেরুলে কলকাতা তোলপাড় হয়ে যাবে। লেফট পার্টিগুলো একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আন্দামানে। রিফিউজি নিয়ে আসা অসম্ভব হয়ে পড়ত। উদ্বাস্তুদের বৃহত্তর স্বার্থে তুমি মোহনবাঁশির রিপোর্টটা পাঠাও নি। কিন্তু প্রচুর লোক যদি হতাহত হয় সেই খবর চেপে রাখা অসম্ভব। আমরা তোমাকে। বার বার এমন খবর গোপন রাখতে অনুরোধ করতে পারি না। তাছাড়া তুমি না জানালেও খবরটা লুকনো থাকবে না। কোনও না কোনওভাবে মেনল্যাণ্ডে সেটা পৌঁছে যাবে। জারোয়ারা বড় আকারে হামলা চালানোর আগেই এর একটা বিহিত করতে হবে।’ বলে জানলার বাইরে দূরমনস্কর মতো তাকিয়ে রইলেন। এ বিনয় লক্ষ করছিল। শেখরনাথ যে জারোয়া হামলার আশঙ্কায় প্রচণ্ড উদ্বিগ্ন এবং জারোয়াদের গায়ে একটা টোকা না মেরেও কিভাবে তাদের ঠেকানো যায় সেই ভাবনায় ডুবে আছেন, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। নিঃশব্দে বসে থাকে বিনয়। আন্দামানে আসার পর থেকে সে একজন নিস্পৃহ সাংবাদিক হয়ে থাকতে পারে নি। এখানকার উদ্বাস্তুদের সুখদুঃখ বর্তমান ভবিষ্যতের সঙ্গেও যেন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছে। তার নিজের ভেতরেও যে প্রবল উৎকণ্ঠা চলছে সেটা টের পাচ্ছিল বিনয়।
হঠাৎ শেখরনাথ ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।–’চল তো বিনয়, দেখি উদ্বাস্তুরা চা রুটি টুটি খেয়ে জমিতে চলে গেছে কিনা–’
দু’জনে যখন বাইরে বেরুবার জন্য পা বাড়িয়েছেন সেই সময় ক্যানেস্তারা পেটানোর তীব্র আওয়াজে জেফ্রি পয়েন্টের প্রায় নিঝুম সকালের নৈঃশব্দ্য খান, খান হয়ে গেল।
‘সর্বনাশ। জারোয়ারা নিশ্চয়ই কলোনির দিকে আসতে শুরু করেছে। ঠিক খবরই দিয়েছিল মাসুদ জগপতরা। চল চল, দেখি উদ্বাস্তুরা মাঠে চলে গেল কিনা—’
বাইরে যেতেই চোখে পড়ল, না উদ্বাস্তুরা এখনও মাঠে গিয়ে কাজ শুরু করে নি। লাইন দিয়ে পুনর্বাসনের কর্মীদের কাছ থেকে সকালের খাবার চা রুটি নিচ্ছে। পরিতোষ অন্যদিনের মতো এই খাদ্য বিতরণ তদারক করছিল। কান ফাটানো ক্যানেস্তারার আওয়াজে খাবার দেবার প্রক্রিয়াটা বন্ধ হয়ে গেল।
পুনর্বাসন আর বন দপ্তরের কর্মীরা বুশ পুলিশের এই আওয়াজ করার কারণটা জানে। উদ্বাস্তুরাও এতদিনে জেনে গেছে।
শেখরনাথ লম্বা লম্বা পায়ে প্রায় দৌড়েই পরিতোষদের কাছে চলে এলেন। তার পেছন পেছন বিনয়ও। তার চোখে পড়ল উদ্বাস্তুদের মুখগুলো ভয়ে ছাইবর্ণ হয়ে গেছে। দিশেহারার মতো তারা উত্তর দিকে তাকিয়ে আছে। চা-রুটি নেবে কি, আতঙ্কগ্রস্তের মতো নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে, ‘আবার জারো (জারোয়া) আইতে আছে। আমরা এইবার শ্যাষ।
শেখরনাথ তাদের বললেন, ‘ভয় পেও না। আজ কেউ জমিতে যাবে না।–পরিতোষ, লা ডিন, ধনপত, বিস্কুট আর গুড়ো দুধের ফাঁকা টিনের বাক্স আছে না? বিদেশ থেকে অনেক চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশন টিনের বাক্স বোঝাই করে পাউডার মিল্ক বিস্কুট ইত্যাদি নানা ধরনের শুকনো খাবার আন্দামানে উদ্বাস্তুদের জন্য পাঠায়। সেগুলোর কথাই জিগ্যেস করলেন শেখরনাথ।
পরিতোষ বলল, ‘মেলা (অজস্র)।’
‘সেগুলো বের করে এনে লাঠি দিয়ে পেটাতে থাকো। মাসুদরা ক্যানেস্তারা পেটাচ্ছে, তোমরাও পেটালে জারোয়ারা পালিয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি কর—’
পুনর্বাসনের কর্মীরা দৌড়ে ব্যারাকের পেছন দিকের গুদাম থেকে কুড়ি পঁচিশটা টিনের বাক্স নিয়ে এল। জঙ্গলে-ঘেরা জেফ্রি পয়েন্টের সব জায়গাতেই গাছের ডালপালার টুকরো পড়ে আছে। সেগুলো তুলে কর্মীরা সমানে টিন পেটাতে শুরু করল। ভয়ার্ত উদ্বাস্তুরা প্রথমটা কুঁকড়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর দু-চারজন কী ভেবে ফাঁকা ক’টা টিন তুলে বেপরোয়া কাঠের টুকরো দিয়ে পিটিয়ে চলল। হয়তো তাদের মনে হয়েছে, জেফ্রি পয়েন্টের এই উপনিবেশ থেকে তো আর কলকাতায় ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। জারোয়ারা যে কোনও দিন, যে কোনও মুহূর্তে হানা দিতে পারে। তাদের গায়ে হাত ঠেকানো যাবে না; রেহাই পাওয়ার একমাত্র উপায়ে নানারকম বিকট আওয়াজ করে, ভয় পাইয়ে জারোয়াদের ফের জঙ্গলে পাঠিয়ে দেওয়া।
বুশ পুলিশরা ক্যানেস্তার পেটাচ্ছে, এদিকে পুনর্বাসনের কর্মী আর উদ্বাস্তুরা ফাঁকা টিন পেটাচ্ছে। প্রচণ্ড আওয়াজ তিন দিকের পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে প্রবল প্রতিধ্বনি তুলছে।
উত্তর দিকে যতদূর জঙ্গল ফেলিং হয়েছে আর যেখানে বুশ পুলিশের উঁচু টঙগুলো দাঁড়িয়ে আছে সেই পেরিমিটার রোড অবধি এখানকার ব্যারাকগুলোর পাশ থেকে মোটামুটি দেখা যায়। হঠাৎ চোখে পড়ল কালো কালো খর্ব চেহারার পঞ্চাশ ষাটজনের এক দঙ্গল জারোয়া তির-ধনুক নিয়ে ওধারের জঙ্গল বেরিয়ে এসে দু’দিক থেকে এত আওয়াজে ভড়কে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওদিকে টঙের মাথা থেকে বুশ পুলিশের দলটা ক্যানেস্তারা বাজাতে বাজাতে সমানে চিৎকারে করে চলেছে, ‘হোঁশিয়ার হোঁশিয়ার—’ তারপরই ওদের মধ্যে দু-একজন আকাশের দিকে বন্দুক উঁচিয়ে সমানে ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করতে লাগল। টিন-ক্যানেস্তারা পেটানোর শব্দের সঙ্গে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ- সব মিলিয়ে এক তুলকালাম কাণ্ড।
জারোয়ারা কী ভাবল তারাই জানে। হয়তো কলোনির জমিতে ঢুকে পড়াটা তাদের পক্ষে নিরাপদ মনে হল না। আচমকা ঝাঁকে ঝাকে তির ছুঁড়ে তারা পলকে গভীর জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল।
আর আওয়াজের প্রয়োজন নেই। টিন-ক্যানেস্তারার শব্দ এবং ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার থেমে গেছে।
শেখরনাথ লক্ষ করেছিলেন, যে উদ্বাস্তুরা আতঙ্ক ঝেড়ে ফেলে টিন বাজিয়েছে তারা হল বৃন্দাবন, হলধর, চন্দ্র জয়ধর, রসময় শীল এবং আরও কয়েকজন। তাদের মধ্যে কী আশ্চর্য, মোহনবাঁশি কর্মকারও রয়েছে। এই তো কদিন আগে মোহনবাঁশির ফুসফুসে জারোয়াদের তির বিধেছিল। মৃত্যুর চোয়ালের ভেতর থেকে যে বেঁচে ফিরেছে সেই লোকটা এর মধ্যে এমন দুর্জয় সাহস পেল কী করে? কোন ভোজবাজিতে? খুব ভাল লাগছিল শেখরনাথের। তিনি প্রায় অভিভূত।।
বৃন্দাবন, মোহনবাঁশি, রসময় শীল, অর্থাৎ যারা টিন পিটিয়ে জারোয়াদের তাড়াতে সাহায্য করেছে, একে একে তাদের সবার কাছে গেলেন শেখরনাথ। প্রত্যেকের কাঁধে হাত দিয়ে বিপুল উৎসাহে বললেন, ‘এমনটাই চাই। দেশের বাড়ি থেকে উৎখাত হয়ে এতদূরে এসে নতুন বসতি গড়ে তুলছ। এটাই হবে তোমাদের নতুন দেশ। তিন দিকে জঙ্গল, জঙ্গলে জারোয়ারা, সমুদ্রে হাঙরের ঝক। এর মধ্যেই বেঁচে থাকতে হবে। সাহস না থাকলে সেটা সম্ভব নয়। সবার পিঠ টিঠ চাপড়ে দিয়ে মোহনবাঁশির কাছে এলেন। তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, তুমি আমাকে অবাক করে দিয়েছে। কর্মকার। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসে এতটা সাহস দেখাতে পারবে ভাবতে পারি নি।
মোহনবাঁশি হাসল। কাকা, দ্যাশ গ্যাছে, ভিটা গ্যাছে, মাটি গ্যাছে। পরান হাতে কইরা কইলকাতা আইছিলাম। হেইহান (সেখান) থনে (থেকে) এই আন্ধারমান দীপি। অহন (এখন) তো আর কইলকাতায় ফিরা যাওনের উপায় নাই। বুকে ডর লইয়া বইয়া (বুকে ভয় নিয়ে বসে থাকলে তো শ্যাষ অইয়া (হয়ে) যামু। আপনেরা খালি (শুধু) আমাগো পাশে থাইকেন। তাইলে (তাহলে) মনের জোর বাড়ব।
‘আমরা সবসময় তোমাদের পাশেই থাকব। বলে অন্য উদ্বাস্তুদের দিকে তাকালেন শেখরনাথ। ‘বেলা অনেকটা চড়ে গেছে। সকাল থেকে অনেক ঝঞ্ঝাট গেল। কারও এখনও সকালের খাবার খাওয়া হয়নি। নাও, নাও, খেয়ে নাও। আজ আর কারও জমির কাজ করার দরকার নেই। কাল থেকে আবার লেগে যেও—’
.
শেখরনাথ আর বিনয়েরও চা’টা খাওয়া হয়নি। সবার সঙ্গে রুটি টুটি খেয়ে শেখরনাথ পরিতোষ বণিককে বললেন, তুমি আমাদের সঙ্গে চল, দরকারী কথা আছে।
পরিতোষ কোনও প্রশ্ন করল না। উৎসুক দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে শেখরনাথদের সঙ্গে তাঁদের ঘরে চলে এল।
শেখরনাথ তার বিছানায় বসলেন, বিনয় বসল নিজের বিছানায় আর পরিতোষ একটু দূরে ঘরের একমাত্র চেয়ারটিতে। শেখরনাথ বললেন, ‘যে কারণে তোমাকে ডেকে আনলাম, এবার সেটা মন দিয়ে শোন।’
কৌতূহল রয়েছে, সেইসঙ্গে দুশ্চিন্তাও–এইরকম একটা মানসিক অবস্থায় শেখরনাথের দিকে। তাকিয়ে রইল পরিতোষ।
শেখরনাথ বললেন, ‘জারোয়ারা কিরকম খেপে আছে, নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ।’
‘হ, কাকা–’ মাথা কাত করল পরিতোষ।
‘আগের যে হামলাটা হয়েছিল, মানে যাতে মোহনবাঁশি জখম হয়, তাতে পাঁচ সাতজন জারোয়া ছিল। কিন্তু আজ চল্লিশ পঞ্চাশজন। লক্ষণটা কিন্তু ভাল নয়—’
পরিতোষ উত্তর দিল না।
শেখরনাথ বলতে লাগলেন, বুশ পুলিশের দুই সিপাই জগপত আর মাসুদ আমাকে খবর দিয়ে গেছে, প্রায়ই দল বেঁধে জারোয়ারা হাতে তিরটির নিয়ে পেরিমিটার রোডের কাছাকাছি চলে আসছে।
‘হ, হেই খবরহান হ্যারা (তারা) আমারেও দিছে।‘
‘এর থেকে কী বোঝা গেল?’
‘আমার মনে লয় (হয়), জারোয়ারা আইজকার লাখান (আজকের মতো) বারে বারে রিফিউজিগো উপুর হামলা চালাইব।’
‘ঠিক ধরেছ।’
‘আজ টিন ক্যানেস্তারা পিটিয়ে, ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করে ওদের তাড়ানো গেছে। কিন্তু জারোয়ারা খুব সম্ভব বুঝে গেছে যতই শূন্যে গুলি ছোঁড়া হোক বা আওয়াজ টাওয়াজ করা হোক, তাদের গায়ে একটা আঁচড়ও কাটা হবে না। তাই ওরা দিন দিন বেপরোয়া হয়ে উঠবে। আজ রিফিউজিরা অনেকটাই সাহস দেখিয়েছে কিন্তু কয়েকজন খুন-জখম হয়ে গেলে তার রি-অ্যাকশন মারাত্মক হয়ে উঠবে। সেজন্যে এখন থেকেই প্রিকশনারি ব্যবস্থা করা দরকার।
‘হেইডা কেমুন কইরা (কেমন করে)?’
‘সুভাষ মজুমদারকে আনাতে হবে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। সুভাষ ছাড়া এই সমস্যার সমাধান আর কারও পক্ষে করা ইমপসিবল—’
‘কুন সুভাষ মজুমদারের কথা কইতে আছেন–অ্যানথ্রোপলিক্যাল ডিপার্টমেন্টের কী?’
‘হ্যাঁ, সে ছাড়া আর কে? আন্দামানে সুভাষ মজুমদার ছাড়া ওই নামের আর কেউ আছে বলে আমার জানা নেই। তোমাদের রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্টের কোনও গাড়িটাড়ি কি এখন জেফ্রি পয়েন্টে আছে?
‘না, নাই তো।’
‘কেন থাকে না? কতরকম এমার্জেন্সি ব্যাপার ঘটতে পারে। যখন তখন তেমন কিছু ঘটলে পোর্টব্লেয়ারে যাওয়া বা খবর দেওয়া দরকার। তোমাদের কর্তা বিশ্বজিৎ রাহাকে বলে পার্মানেন্টলি এখানে একটা গাড়ি রাখার ব্যবস্থা করবে।’
‘কাকা, আপনে যদিন রাহা সাহেবরে কইয়া দ্যান, তাইলে কামটা তরতরি অইয়া যাইব।‘
‘আমি বাইরের লোক, এসব তো মেনলি তোমাদের পুনর্বাসন ডিপার্টমেন্টের কাজ। বিশেষ করে তুমি হলে এই জেফ্রি পয়েন্টের কর্তা। তোমারই করা উচিত।’
ঢোক গিলে ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে পরিতোষ বলল, কেডা কয় আপনে বাইরের মানুষ। আপনের লাখান (মত) রিফিউজিগো বান্ধব আর কেও (কেউ) এই আন্দামানে নাই। হেয়া (তা) ছাড়া—’
‘তা ছাড়া কী?’
‘আপনে কিছু কইলে চিফ কমিশনার থিকা (নেবে) সৰ্গলে (সবাই) শোনে। ইউ আর মোস্ট র্যাসপ্যাক্টেড (রেসপেক্টেড) পার্সন অফ দিজ আইল্যাণ্ডস। আমি অইলাম (হলাম) চুনা পুডি (পুঁটি)। আমার কথায় বড় কত্তারা কি কান দ্যায়? এক কান দিয়া হুনব (শুনবে), আরেক কান দিয়া বাইর কইরা দিব। আপনে কিছু কইলে হার (তার) ওজন কত! যা করনের আপনেরেই করতে অইব (হবে) কাকা।’
একটু মজাই হয়তো পেলেন শেখরনাথ, চোখ ছোট করে বললেন, ‘তোষামুদিটা ভালই শিখেছ। এমন মিন মিন করলে চলবে না। নিজের জন্যে তুমি কিছু চাইছ না। চাইছ উদ্বাস্তুদের জন্যে। এতগুলো মানুষকে কলকাতা থেকে এখানে টেনে আনা হয়েছে। তাদের জন্যে যা যা করা দরকার করবে, জোর করে সব আদায় করে নেবে। বড় কর্তাদের ভয়ে কুঁকড়ে থাকলে চলবে না।’
মুখ নিচু করে চুপ করে রইল পরিতোষ। বোঝা গেল, আন্দামান অ্যাডমিনিস্টেশনের হর্তাকর্তা বিধাতাদের কাছে উঁচু গলায় উদ্বাস্তুদের স্বার্থে কিছু দাবি করার মতো বুকের পাটা তার নেই। অথরিটি যে নির্দেশ বা হুকুম দেবে, মুখ বুজে তা-ই তালিম করে যাবে। ( পরিতোষের মতো একজন তুচ্ছ এমপ্লয়ির নিরুপায়তা বুঝলেন শেখরনাথ। তার পিঠে একটা হাত রেখে নরম গলায় বললেন, ঠিক আছে, যা করার আমিই করব। মনে সাহস আনন। ওপর থেকে অর্ডার এল আর তুমি চোখকান বুজে তাই করে যাবে সেটা হয় না। পুনর্বাসনের কাজটা হল মানুষ নিয়ে। এই জঙ্গলে কখন তাদের কোন বিপদের মুখে পড়তে হবে, আগেভাগে তো জানা যায় না। আমি তো চিরকাল এই জেফ্রি পয়েন্টে পড়ে থাকব না; তোমাকেই কিন্তু সব কিছু করতে হবে। যদি জোর করতে হয় তাই করবে। তোমার অথরিটিকে বোঝাতে হবে নিজের স্বার্থে তুমি কিছুই করছ না। যা করছ দেশ-হারানো, জন্মভূমি থেকে উৎখাত, একদল মানুষের জন্যে। এমনভাবে জোর দিয়ে বলবে যাতে কর্তারা সেটা ভাল করে বুঝতে পারে। দেখবে তাতে কাজ হবে।
এবারও উত্তর দিল না পরিতোষ। শেখরনাথ টের পেলেন তার দীর্ঘ বক্তৃতাও পরিতোষকে চনমনে করে তোলা তো দূরের কথা, প্রশাসনের কর্তাদের সম্পর্কে তার ভয়টাকে এতটুকু নড়াতে পারে নি। সেটা জগদ্দল পাথরের মতো তার ওপর চেপে আছে। তিনি বললেন, ঠিক আছে, আপাতত আমিই সব ব্যবস্থা করছি। রিহ্যাবিলিটেশনের গাড়ি টাড়ি তো কিছুই নেই বললে, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কোনও জিপ বা ট্রাক আছে?
এবার মুখ খুলল পরিতোষ।–’একহান (একটা) জিপ আর একহান লরি আছে।‘
‘আমি বিশুকে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের আজীব সিংকে বলবে তার জিপটা কয়েক ঘন্টার জন্যে আমার চাই। তোমাদের ডিপার্টমেন্টের কারওকে আমার চিঠিটা দিয়ে এখনই বিশুর কাছে পাঠিয়ে দেবে। আজীব সিংকে বলবে, যে যাচ্ছে ব্যম্বু ফ্ল্যাটের জেটিতে তাকে পৌঁছে দিয়েই যেন ওদের জিপ চলে আসে। তোমাদের এমপ্লয়িটিকে পাঠাবার ব্যবস্থা বিশুই করে দেবে। একটু বোসো–’
শেখরনাথ ক্ষিপ্র হাতে একটা চিঠি লিখে খামে ভরে আঠা দিয়ে সেটার মুখ আটকে দিলেন। তার ওপর বিশ্বজিৎ রাহার নাম লিখলেন।
চিঠি নিয়ে পরিতোষ চলে গেল।
প্রাচীন বিপ্লবীটিকে যত দেখছে, ততই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে বিনয়ের। দেশকে ভালবেসে একদিন ইংরেজের হাতে কত নিদারুণ নির্যাতন সহ্য করেছেন, সেলুলার জেলের সলিটারি সেলে কতদিন তাঁকে কাটাতে হয়েছে। জেলরের হুকুমে ‘টিকটিকি’তে চড়িয়ে পাঠান আর জাঠ পেটি অফিসার কি টিণ্ডালরা চাবুক মেরে মেরে তাঁকে রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে। দেশভাগ আর স্বাধীনতার পর সেই অদম্য স্বাধীনতা-সংগ্রামীর অফুরান ভালবাসা এসে পড়েছে পূর্ব পাকিস্তানের ছিন্নমূল মানুষগুলোর ওপর। যতদিন না তারা পাহাড় জঙ্গল সমুদ্রে-ঘেরা এই সৃষ্টিছাড়া জেফ্রি পয়েন্টে মনের মতো করে নির্বিঘ্নে তাদের উপনিবেশ গড়ে তুলছে তার ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই, স্বস্তি নেই। তার সর্বক্ষণের শ্বাসপ্রশ্বাসে জড়িয়ে গেছে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বস্বখোয়ানো এই মানুষগুলো। অন্যদিকে আন্দামানের প্রাচীন জনজাতি জারোয়াদের জন্যও তাঁর উদ্বেগের অবধি নেই। এই অরণ্যবাসী মানুষগুলোর যাতে লেশমাত্র ক্ষতি না হয় সেদিকেও তার তীক্ষ্ণ নজর। তিনি চান সবাই পাশাপাশি থাকুক। সুষ্ঠু, বিঘ্নহীন সহাবস্থানটাই তার একান্ত কাম্য।
বিনয় ধন্দে পড়ে গিয়েছিল। চব্বিশ ঘন্টা বুশ পুলিশের নজরদারি সত্ত্বেও জারোয়ারা আজ বেপরোয়া হামলা চালালো। শেখরনাথের আশঙ্কা তারা এরকম বার বার হানা দেবে। ক্যানেস্তারা পিটিয়ে আর ব্লাঙ্ক ফায়ার করে শেষ পর্যন্ত তাদের রোখা যাবে না। এই যখন অবস্থা, তখন অ্যানথ্রোপলজিকাল ডিপার্টমেন্টের জনৈক সুভাষ মজুমদার জেফ্রি পয়েন্টে এসে কোন ভোজবাজিতে এই মহা বিপজ্জনক সমস্যার সমাধানটা কী করে করবে, সে ভেবে পেল না। তার মনে যে সংশয় দেখা দিয়েছে সেটা বলেও ফেলল।
শেখরনাথ জানলার বাইরে তাকিয়ে কিছু ভাবছিলেন। চোখ ফিরিয়ে বললেন, ‘নৃতত্ত্ব বিভাগের এই বিজ্ঞানীটি আন্দামানের আদিম বাসিন্দা ওঙ্গে, সেস্টিনালিজ, গ্রেট আন্দামানিজ আর জারোয়াদের নিয়ে অনেক কাজ করেছে। বিশেষ করে জারোয়াদের নিয়ে দূরে বসে ব্রিটিশ অ্যানথ্রোপলজিস্টদের বইয়ের পাতা ঘেঁটে থিওরিটিক্যাল রিসার্চ নয়, রীতিমতো ওদের সঙ্গে মিশে প্রচুর গবেষণার কাজ করে চলেছে। সাউথ আর মিডল আন্দামানের জারোয়াদের সঙ্গে সুভাষই একমাত্র ইন্ডিয়ান অ্যানথ্রোপলজিস্ট যে কিনা যোগাযোগ করতে পেরেছে। জারোয়াদের ভাষা, জীবনযাত্রার ধরন, প্রায় সবটাই জানে। ব্রিটিশ অ্যানথ্রোপলজিস্টরা জারোয়াদের সঙ্গে কতটা কনট্যাক্ট করতে পেরেছিল আমার স্পষ্ট ধারণা নেই। তাদের দু-চারটে লেখা পড়েছি– এইমাত্র। কিন্তু সুভাষ যে কত বড় কাজ করে চলেছে, ভাবা যায় না।’
বিনয়ের ধন্দটা কিছুতেই কাটছে না।-–’কাকা, বুঝতে পারছি না, সুভাষ মজুমদার এসে কিভাবে হিংস্র জারোয়াদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করবেন।’
শেখরনাথ হাসলেন, ‘কৌশলটা আমারও ঠিক জানা নেই। সে আসুক, তখন দেখতে পাবে।‘
‘একটা কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।‘
‘কী কথা?’
‘ওঙ্গেরা শুনেছি খুব নিরীহ ধরনের। তাদের নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। গ্রেট আন্দামানিজরা রেসিয়ালি পিওর নয়। নানা রক্তের মিশ্রণে তাদের চেহারা টেহারাও পালটে গেছে। সংখ্যায় তারা নাকি মাত্র পঁচাত্তর জনে এসে ঠেকেছে। তাদের সম্বন্ধে অ্যানথ্রোপলজিস্টদের বিশেষ ইন্টারেস্ট নেই। কিন্তু জারোয়ারা তো ভীষণ হিংস্র। সো-কলড সভ্য জগতের মানুষজনকে তারা সহ্য করতে পারে, ধারেকাছেও ঘেঁষতে দেয় না। সুভাষ মজুমদার তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন কী করে?’
‘আমি যখন চিঠি পাঠিয়েছি আর জেফ্রি পয়েন্টে এত বড় একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে তখন সে চুপচাপ পোর্ট ব্লেয়ারে বসে থাকতে পারবে না। ঠিক চলে আসবে। সে এলে তাকেই জিগ্যেস করে তোমার প্রশ্নের উত্তরগুলো জেনে নিও।’
বিনয় আর কিছু বলল না। অফুরান কৌতূহল নিয়ে সুভাষ মজুমদারের জন্য উদগ্রীব অপেক্ষা করা ছাড়া এখন আর তার কিছু করার নেই। বিচিত্র ওই নৃতত্ত্ববিদকে দেখার জন্য সে ব্যগ্র হয়ে থাকবে।
.
৪.১৯
কাল জেফ্রি পয়েন্টের আমিন লা-ডিনকে শেখরনাথের চিঠি দিয়ে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের একটা জিপে পাঠিয়ে দিয়েছিল পরিতোষ বণিক। জিপটা লা-ডিনকে পোর্টব্লেয়ারের এধারের ব্যাম্বু ফ্ল্যাটে জেটিতে নামিয়ে দিয়ে কালই ফিরে এসেছিল।
আজ অন্য একটা জিপে লা-ডিন ফিরে এল। জিপটা সোজা উদ্বাস্তুদের জন্য যে ব্যারাকগুলো তোলা হয়েছে সেখানে এসে থামল।
কাল সকালের দিকে জারোয়ারা দল বেঁধে উদ্বাস্তুদের কলোনিতে ভয়াবহ হামলা চালিয়েছিল। শেখরনাথ উদ্বাস্তুদের জমিতে গিয়ে কাজ করতে বারণ করেছিলেন; তাই জমি সাফাই বন্ধ ছিল। উদ্বাস্তুরা ব্যারাকের চারপাশে এধারে ওধারে থোকায়-থোকায় বসে বা ঘোরাঘুরি করে দিনটা কাটিয়ে দিয়েছে। আজ কিন্তু জেফ্রি পয়েন্টের ছবিটা অন্যরকম। সকাল হতে না-হতেই চা-রুটি খেয়ে ছিন্নমূল মানুষগুলো দা-কুড়াল, কোদাল-টোদাল নিয়ে জমিতে নেমে পড়েছে। আসলে জারোয়াদের ভয়টা তারা কাটিয়ে উঠছে। শুধু সকালের দিকেই নয়। দুপুরে খাওয়াদাওয়া চুকিয়ে ফের জমির আগাছা বাছাই শুরু করেছে। এই সাহস দেখানোটা সত্যিই বিরাট সুলক্ষণ।
বিকেলবেলা বিনয়কে সঙ্গে নিয়ে শেখরনাথ ব্যারাকগুলোর কাছাকাছি রসময় শীলের জমিতে তাদের কাজকর্ম দেখছিলেন। কিন্তু নজর ছিল পুব দিকের পাহাড়ের গায়ে যে পাথর-কাটা রাস্তাটা জেফ্রি পয়েন্টের দিকে ঢাল বেয়ে নেমে এসেছে সেই দিকে। জিপটাকে ব্যারাকের সামনে এসে থামতে দেখে বিনয়কে বললেন, ‘চল, সুভাষরা এসে গেছে।
লম্বা লম্বা পা ফেলে শেখরনাথরা জিপটার কাছে চলে এলেন। ততক্ষণে লা-ডিন এবং আরও একজন নেমে পড়েছেন। অচেনা, আধবয়সি মানুষটিচল্লিশ-পঞ্চাশের মতো বয়স, ছিপছিপে বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, মাঝারি হাইট, পরনে ঢোলা ফুলপ্যান্ট আর শার্ট, পায়ে চপ্পল, চোখে পুরু ফ্রেমের। চশমা–তিনিই যে সুভাষ মজুমদার বুঝতে পারল বিনয়। যে গাড়িটা চালিয়ে এনেছে সেও নেমে পড়েছে।
শেখরনাথ বললেন, ‘যাক, তুমি এসে গেছ। ভেবেছিলাম আজ দুপুরের আগে আগে চলে আসবে। দেখলাম সেটা মিলে গেছে।’
প্রাচীন বিপ্লবীটির পা ছুঁয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালেন সুভাষ। বললেন, ‘কাল রাহাসাহেব (বিশ্বজিৎ রাহা) যখন গাড়ি পাঠিয়ে আমাকে তার বাংলোতে ডেকে নিয়ে জানালেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। জেফ্রি পয়েন্টে যেতে হবে, আমার আপত্তি বা অসুবিধে আছে কিনা। বললাম, কোনওটাই নেই। শুধু আমাদের অ্যানথ্রোপলজিকাল ডিপার্টমেন্টের বড় কর্তা ডাক্তার শ্যামচৌধুরিকে একবার জানাতে হবে। রাহা সাহেব চিঠি লিখে তার অনুমতি আনিয়ে নিলেন। কিন্তু তখন অনেকটা রাত হয়েছে। ততক্ষণে ব্যাম্বু ফ্ল্যাট-চ্যাথাম ফেরি সারভিস বন্ধ হয়ে গেছে। আসার উপায় ছিল না।’
আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন শেখরনাথ। কিছু বললেন না।
সুভাষ মজুমদার বলতে লাগলেন, ‘সকালে উঠেই যে চলে আসব তার উপায় ছিল না। আপনি জেফ্রি পয়েন্টের জন্যে পার্মানেন্টলি একটা গাড়ি চেয়েছেন। গাড়ি আর ড্রাইভারের ব্যবস্থা করতে বেশ দেরি হয়ে গেল রাহা সাহেবের। তারপর সেই গাড়ি চ্যাথাম জেটিতে এনে স্টিমারে তুলে ব্যাম্বু ফ্ল্যাটে নামাতে বেশ খানিকটা সময় লাগল। এতসব হাঙ্গামার পর তবে আসতে পারলাম।’
‘ঠিক আছে, রাস্তায় অনেক ধকল গেছে। এখন চল আমাদের সঙ্গে। আজ আর তো কিছু করা যাবে না। সন্ধে হতে বেশি দেরি নেই। রাতটা ভাল করে রেস্ট নাও। যা করার কাল কোরো।‘
‘হ্যাঁ, তাইই করতে হবে। সুভাষ শেখরনাথের সঙ্গে কথা বলছিলেন ঠিকই, কিন্তু তার চোখ বার বার এসে পড়ছিল বিনয়ের দিকে।–’আপনি নিশ্চয়ই বিনয় বসু। বলে হাতজোড় করলেন।‘
বিনয়ও হাতজোড় করে বলল, হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। নিশ্চয়ই আমার কথা বিশ্বজিৎবাবুর কাছে শুনেছেন।
‘হ্যাঁ। আপনি ‘নতুন ভারত’ কাগজের সাংবাদিক। আন্দামানে রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশন কভার করতে এসেছেন আর এখন জেফ্রি পয়েন্টে আছেন।‘
বিনয় হাসল। কিন্তু অবাক বিস্ময়ে ভাবতে লাগল ‘এই মানুষটি কী করে যে জারোয়াদের সমস্যাটার সুরাহা করবেন, কে জানে।‘
শেখরনাথ তাড়া দিলেন।–-‘আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকে না। চল–চল—’
সুভাষ মজুমদার বললেন, ‘জিপে অনেক কিছু নিয়ে এসেছি, নামাতে হবে।‘
পরিতোষ এবং জেফ্রি পয়েন্ট রিহ্যাবিলিটেশনের বেশ কয়েকজন কর্মী সুভাষ মজুমদারদের দেখে চলে এসেছিল। তারা চুপচাপ একধারে দাঁড়িয়ে আছে। শেখরনাথ পরিতোষকে বললেন, ‘সুভাষের মালপত্র নামিয়ে আমাদের ঘরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর। আর যে ড্রাইভারটি গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এসেছে সে পার্মানেন্টলি এখানে থাকবে। তার থাকার অ্যারেঞ্জমেন্টও করে দেবে। আর হ্যাঁ, বিশু ওই জিপটা পাঠিয়ে দিয়েছে। এখন থেকে জেফ্রি পয়েন্ট সেটলমেন্টের কাজে লাগানো হবে।
পরিতোষ ব্যস্ত হয়ে পড়ল।–’আমি অহনই (এখনই) হগল (সকল) বন্দোবস্ত করতে আছি।‘
শেখরনাথ বললেন, ‘সুভাষ সেই কখন পোর্টব্লেয়ার থেকে বেরিয়েছে। ওর জন্যে চা আর কিছু খাবারও পাঠাবে। লা-ডিন আর ড্রাইভারটিকেও দেবে।‘
‘হ। নিয্যস (নিশ্চয়ই)।‘
শেখরনাথ সুভাষকে নিয়ে তাদের ঘরে চলে গেলেন। বিনয়ও তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে এল। সুভাষ মজুমদার সম্বন্ধে তার বিপুল আগ্রহ।
ঘরে এসে তিনজন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে তক্তপোষের বিছানা আর চেয়ারে বসে পড়ল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পুনর্বাসন দপ্তরের দু’জন কর্মী তিন চারটে চটের ব্যাগ বোঝাই জিনিস আর একটা চামড়ার স্যুটকেস নিয়ে এল। তার পরে-পরেই পরিতোষ এবং ধনপত সিং একটা বড় কাঠের পরাতে তিনজনের মতো চা আর প্রচুর দামি দামি বিস্কুট এনে টেবিলের ওপর রাখল।
হঠাৎ কিছু মনে পড়ে গেল শেখরনাথের। বললেন, একটা কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। সুভাষ যে ক’দিন জেফ্রি পয়েন্টে আছে আমাদের ঘরেই থাকবে। ওর জন্যে এখানে একটা তক্তপোষ আর বিছানা-টিছানা তোমার লোকদের দিয়ে যেতে বলবে। মশারিও চাই। নইলে রাত্তিরে মশা আর বাঢ়িয়া পোকায় ছিঁড়ে খাবে।
ঘাড় হেলিয়ে পরিতোষ চলে গেল।
চা খেতে খেতে এলোমেলো কিছু কথা হল। বিনয় নীরব শ্রোতা। সে জানতে পারল সুভাষ অবিবাহিত। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এখানকার অ্যানথ্রোপলজিকাল ডিপার্টমেন্টটাকে ঢেলে সাজানো হয়েছে। প্রথম থেকেই সুভাষ আন্দামানের জনজাতিগুলোর ওপর একাগ্রভাবে গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। একসময়, সেই নাইনটিনথ সেঞ্চুরির শেষাশেষি অবধি আন্দামানে তেরোটি উপজাতি ছিল। খর্বকায়, নিগ্রো গোষ্ঠীর মানুষজন। ন’টা গোষ্ঠী বিলুপ্ত হয়ে গেছে। টিমটিম করে চারটে কোনও রকমে টিকে আছে। ওঙ্গে, জারোয়া, গ্রেট আন্দামানিজ আর সেন্টিনালিজ। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের সবচেয়ে দক্ষিণে যে দ্বীপটা আছে তার নাম লিটল আন্দামান। ছোট্ট দ্বীপ, আয়তন মাত্র উনপঞ্চাশ বর্গমাইল। এখানেই থাকে ওঙ্গেরা। সংখ্যায় তারা মাত্র চারশো সাতাশি। এরা খুবই নিরীহ, শান্ত। এদের আদি ইতিহাস থেকে সামাজিক আচার আচরণ, ভাষা, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি প্রচুর খুঁটিনাটি তথ্য জেনে নিয়েছে সুভাষ। এই নিয়ে অনেকটাই লিখে ফেলেছে। দু-এক মাসের ভেতর বাকিটা শেষ করে ফেলবে। গ্রেট আন্দামানিজদের সম্পর্কে নৃতাত্ত্বিকদের আপাতত বিশেষ আগ্রহ নেই। কেন না, তারা উপজাতি হিসেবে বিশুদ্ধ নয়। অন্য রক্তের সংমিশ্রণের ফলে তাদের চেহারা এবং আকৃতিও পালটে গেছে। কমতে কমতে ওদের সংখ্যা এখন মাত্র পঁচাত্তর জন। গ্রেট আন্দামানিজরা কয়েক বছরের মধ্যেই লুপ্ত হয়ে যাবে। বাকি রইল জারোয়া আর সেন্টিনালিজরা। দক্ষিণ আর মধ্য আন্দামানের উত্তর আর পশ্চিম দিকের গভীর অরণ্যে থাকে জারোয়ারা। আর মিডল এবং সাউথ আন্দামানের পশ্চিম দিকে আরও দুটো দ্বীপ আছে। সাউথ সেন্টিনেল আর নর্থ সেন্টিনেল। এই দুই দ্বীপের বাসিন্দারা হল সেন্টিনালিজ। জারোয়া আর সেন্টিনালিজরা ভীষণ হিংস্র। বাইরে থেকে কেউ তাদের এলাকায় এলে একেবারেই সহ্য করতে পারে না।
জারোয়াদের সঙ্গে মোটামুটি অনেকটাই যোগাযোগ করতে পেরেছেন সুভাষ। কিন্তু সেন্টিনালিজদের ধারে কাছে ঘেঁষা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। অ্যানথ্রোপলজিকাল ডিপার্টমেন্টের স্টিমলঞ্চ ওই দুটো দ্বীপের কাছে গেলেই সেন্টিনালিজরা ঝাঁকে ঝাঁকে তির চালাতে শুরু করে। ওদের বিশ্বাসভাজন হয়ে বন্ধুত্ব করে তথ্য জোগাড় করা খুবই কঠিন, সেজন্য অনেক সময় লাগবে।
এই ধরনের কথাবার্তার ফাঁকে একসময় আসল প্রসঙ্গে চলে এলেন শেখরনাথ। এখানকার কথা তো বিশুর কাছে শুনেছ। আমরা ভীষণ সংকটে আছি।
আন্দামানের উপজাতিরা যে সুভাষ মজুমদারকে কতটা আবিষ্ট করে রেখেছে, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল। একেবারে মগ্ন হয়ে তিনি ওদের সম্বন্ধে বলে যাচ্ছিলেন। এবার একটু অপ্রস্তুত হলেন। ব্যস্তভাবে বললেন, ‘হ্যাঁ হ্যাঁ, মিস্টার রাহার কাছে সব শুনেছি। আর সেই জন্যেই তো আমার এখানে আসা।’
‘দেখ সুভাষ, যেভাবে জারোয়ারা হামলা চালাচ্ছে তাতে জেফ্রি পয়েন্ট সেটলমেন্টের পক্ষে সেটা ভীষণ ক্ষতিকর। আমরা তোমার দিকে তাকিয়ে আছি।’
সুভাষ মজুমদার হাসলেন।–’আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করব। আসলে কি জানেন কাকা—’
শেখরনাথ উৎসুক হলেন, তবে কোনও প্রশ্ন করলেন না।
সুভাষ থামেন নি।–’অনেকদিন আগে ইংরেজরা জারোয়াদের জংলি বর্বর তা লাগিয়ে সাঁইত্রিশজনকে ধরে এনে পোর্টব্লেয়ারের এবারডিন মার্কেটের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মেরেছিল। সেই থেকে বংশপরম্পরায় সভ্য জগতের মানুষজন দেখলে তারা খেপে ওঠে।‘
শেখরনাথ বললেন, ‘গুলি করে যে ইংরেজরা মেরেছিল তা জানি। কিন্তু সেই কারণে এত বছর বাদেও বংশধরেরা রাগ পুষে রেখেছে সেটা জানা ছিল না।‘
‘তা ছাড়া রাগের আরও একটা বড় কারণ তো আপনি জানেন।‘
‘হ্যাঁ, জানি। জঙ্গল রিক্লেম করে ওদের এরিয়া ছোট করে দেওয়া হচ্ছে। এটা ওরা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। চিফ কমিশনারের কাছে অ্যাপিল করেছি, অ্যাট লিস্ট জেফ্রি পয়েন্টের উত্তর দিকটায় জঙ্গল ফেলিং বন্ধ করা হোক। তিনি পালটা প্রশ্ন করলেন, দলে দলে ডি পি ফ্যামিলিগুলো কলকাতা থেকে আসছে। জঙ্গল নিমূল না করলে জমি কোথায় পাওয়া যাবে? আর জমি না পেলে এত মানুষের রিহ্যবিলিটেশন হবে কী করে? ব্যাপারটা অস্বীকার করা যায় না। তবু আমি জেদ ধরেছিলাম, উত্তর দিকটা বাদ দিয়ে পুব আর পশ্চিম দিকের জঙ্গল কাটা হোক। তাকে কোনও মতেই রাজি করাতে পারি নি। একটু চুপ করে থেকে ফের শুরু করলেন, ‘আন্দামান অ্যান্ড নিকোবর আইল্যান্ডস-এর অথরিটির কথায় যুক্তি আছে। সবই বুঝতে পারছি। কিন্তু জারোয়াদের শান্ত করতে না পারলে তো মহাবিপদ।‘
সুভাষ মজুমদার হাসলেন।–-‘সেইজন্যেই তো আপনি আমাকে এখানে ডেকে এনেছেন। আমার দিক থেকে চেষ্টার ত্রুটি হবে না।‘
আন্দামানের আদিম জনগোষ্ঠীগুলো সম্পর্কে সুভাষের কতটা গভীর জ্ঞান, অবাক হয়ে ভাবছিল বিনয়। সে আর মুখ বুজে থাকতে পারল না। অনন্ত এক কৌতূহল তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল।–’শান্ত করতে হলে ওদের কাছে তো যেতে হবে।‘
হাসিটা সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল সুভাষের। বললেন, ‘তা তো যেতেই হবে। নইলে বোঝাব কী করে?’
বলে কী লোকটা? বিস্ময়ের অবধি নেই বিনয়ের।–‘কিন্তু—’
‘আপনি কী বলতে চাইছেন, বুঝতে পারছি। জারোয়ারা সো-কলড সিভিলাইজড পিপলকে তাদের ত্রি-সীমানায় ঘেঁষতে দেয় না, তাই তো?’
‘হ্যাঁ—‘
যেন জলভাতের মতো ব্যাপার, এমন একটা ভঙ্গিতে সুভাষ মজুমদার বললেন, ‘আমাকে ওদের সঙ্গে দেখা করে কথা বলতেই হবে।‘
‘আপনি কি ওদের ভাষা জানেন?’
‘অনেকটাই জানি।‘
বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকে বিনয়। তার মনোভাবটা আন্দাজ করে নিয়ে সুভাষ মজুমদার বললেন, ‘স্বাধীনতার কয়েক বছর আগে সেই ইংরেজ আমলে দুটো জারোয়া ছেলেকে ব্রিটিশ পুলিশ ধরে ফেলেছিল। না, সেই নাইনটিনথ সেঞ্চুরিতে জারোয়াদের যেভাবে মার্ডার করা হয়েছিল এদের তা করা হয় নি। অ্যানথ্রোপলজিকাল স্টাডির জন্যে ছেলে দু’টোকে, তখন দশ বারো বছর বয়স ছিল, কার নিকোবর আইল্যান্ডে নিয়ে রাখা হয়। আমি পোর্টব্লেয়ারে আসার পর নিকোবরে গিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা করি। কাজ চালানোর মতো ইংরেজি সেই আমলের অ্যানথ্রোপলজিস্টরা ওদের শিখিয়েছিলেন। জঙ্গলে প্রায় অর্ধ-উলঙ্গ হয়ে ওরা থাকত। নিকোবরে পরত প্যান্ট-শার্ট। এদের সঙ্গে প্রথম দিকে একটানা চার মাস কাটাই। তারপর কিছুদিন পর পর যেতাম, এখনও অন্য সব কাজের ফকে সময় পেলেই চলে যাই। জঙ্গলে যেসব আদিবাসীরা থাকে, তাদের আমরা তথাকথিত সভ্য জগতের মানুষ জংলি, অসভ্য–এইসব তা দিয়ে থাকি। কিন্তু ছেলে দুটো যথেষ্ট মেধাবী, খুবই ইনটেলিজেন্ট। নিকোবরের একটা স্কুলে তারা পড়ছে। যে কোনও বিষয় চট করে ধরে ফেলতে পারে। মেমোরিও যথেষ্ট শার্প। ওদের কাছ থেকে জারোয়াদের ভাষাটা মোটামুটি শিখে ফেলি। ওদের সমাজ সম্পর্কে, জীবনযাপন সম্পর্কে একটা ভাল ধারণাও তৈরি হয়ে যায়।’ একনাগাড়ে বলে যাবার কারণে কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার আরম্ভ করলেন, ‘আপনাদের বলেছি, সাউথ আন্দামানের পশ্চিম দিকের ঘন জঙ্গলে যেমন জারোয়ারা থাকে, মধ্য আন্দামানের পশ্চিম দিকের জঙ্গলেও ওদের অনেকেই থাকে। নিকোবরের ওই ছেলে দু’টির কাছ থেকে ওদের যে ভাষা, হাব-ভাব, আচার-আচরণ শিখেছিলাম সেটুকু পুঁজি করে মিডল আন্দামানের জঙ্গলে জারোয়াদের মধ্যে চলে যাই। ভয় যে করে নি তা নয়। কিন্তু নৃতাত্ত্বিক স্টাডি তো ঘরে বসে করা যায় না। সব উপজাতিই ওঙ্গেদের মতো নিরীহ, শান্ত নয়। অনেকেই অত্যন্ত হিংস্র। ঝুঁকি না নিলে তাদের সম্বন্ধে গভীরভাবে জানব কী করে? মিডল আন্দামানে গিয়ে জারোয়াদের সম্বন্ধে আরও অনেক কিছুই জানতে পারি যা আমার গবেষণার পক্ষে খুবই কাজে লেগেছে।’
বিনয় জিগ্যেস করল, ‘জারোয়ারা যেরকম ভয়ঙ্কর টাইপের, মিডল আন্দামানে আপনাকে বিপদের মধ্যে পড়তে হয় নি?’
সুভাষ মজুমদার বেশ মজাই পেলেন যেন।–’তা একটু আধটু পড়তেই হয়েছে। উটকো একটা প্যান্ট-শার্ট পরা লোক তাদের মধ্যে এসে পড়েছে, চট করে কি তাকে মেনে নিতে চায়? সন্দেহ হওয়াটা স্বাভাবিক। তারপর আমার মুখে ওদের ভাষাটা শুনে ধীরে ধীরে বুঝতে পারে আমি কোনও রকম ক্ষতি করতে যাই নি। একবার নয়, বেশ কয়েক বার যাতায়াতের ফলে ওদের সঙ্গে বেশ বন্ধুত্বই হয়ে যায়। জারোয়াদের সম্বন্ধে আরও অনেক কিছুই জানতে পারি। আমার সেই জ্ঞানটুকু নিয়ে জেফ্রি পয়েন্টে এসেছি। আমি চূড়ান্ত আশাবাদী। আমার ধারণা, সাউথ আন্দামানের জারোয়াদের সঙ্গে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে আসতে পারব। জঙ্গলেই থাকুক আর পাহাড়েই থাকুক–মানুষ তো। মানুষের সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার করলে যথেষ্ট কাজ হয় বলেই আমার বিশ্বাস। তারপর দেখা যাক।‘
.
শেখরনাথদের ঘরেই বাড়তি একটা তক্তপোষ এনে বিছানা-টিছানা পেতে সুভাষ মজুমদারের থাকার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল পরিতোষ বণিকরা। রাত্তিরে খাওয়া দাওয়ার পর বেশি রাত পর্যন্ত কেউ জেগে রইলেন না। সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন।
পরদিন সকালে সবার আগে ঘুম ভাঙল সুভাষ মজুমদারের। তিনি শেখরনাথ এবং বিনয়কেও জাগিয়ে দিলেন। বললেন, ‘কাকা, আমি কিন্তু একটু পরেই জঙ্গলে গিয়ে ঢুকব।‘
‘হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার চা আর সকালের খাবারের ব্যবস্থা করছি।‘ শেখরনাথ বেরিয়ে গিয়ে হাঁকডাক করে পরিতোষ এবং পুনর্বাসনের অন্য কর্মীদের ঘুম থেকে তুলে রুটি, আলুভাজা আর হালুয়া,বানাতে বললেন। জেফ্রি পয়েন্টে সবার সকালের খাবার হল আগের দিনের তৈরি বাসি রুটি, গুড় আর বিদেশের চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশনগুলো থেকে পাঠানো পাউডার মিল্ক গুলে জ্বাল দিয়ে এক গেলাস করে গরম দুধ। এমনকি রিহ্যাবিলিটেশনের যত বড় অফিসারই আসুন না কেন, বাসি রুটি টুটি দিয়ে তাঁদেরও ব্রেকফাস্ট করতে হয়। কিন্তু যে মানুষটা জীবনের প্রচন্ড ঝুঁকি নিয়ে জারোয়াদের এলাকায় যাবে, তাকে ওই ধরনের খাবার দিতে চান নি শেখরনাথ।
কয়েক মিনিটের ভেতর সুভাষের জন্য টাটকা খাবার তৈরির তোড়জোড় শুরু হল। ইতিমধ্যে উদ্বাস্তুরা জেগে উঠেছে। তাদের আগাছা সাফ করার জন্য নিজের নিজের জমিতে যেতে হবে। তাই তুমুল ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে।
উপসাগর থেকে মুখটুখ ধুয়ে এসে সুভাষ মজুমদার তার ব্যাগগুলো বেশ ভাল করে গুছিয়ে নিলেন। সেগুলোতে রয়েছে নানা রকমের বিস্কুট, লাড়ু আর গজা জাতীয় শুকনো মিষ্টি। আর আছে। লাল, নীল, হলুদ, সবুজ–এমন নানা রঙের কাপড়ের টুকরো। তিন চার ফুটের মতো লম্বা, ফুট দুয়েক চওড়া।
গোছগাছ হয়ে গেলে চা-খাবার টাবার খেয়ে সারা গায়ে হালকা নীল রঙের লোশন মেখে নিলেন সুভাষ মজুমদার। বিনয় একদৃষ্টে তাকে লক্ষ করছিল। এই বিশেষ লোশন মাখার কারণ জানে সে। জঙ্গলে ঢুকলে গাছের মাথা থেকে থোকায় থোকায় জোঁক গায়ের ওপর এসে পড়ে। এই তরল পদার্থটির মধ্যে রাসায়নিক এমন কিছু তীব্র জিনিস মেশানো থাকে যাতে গায়ে পড়েই জোঁকেরা শুকনো পাতার মতো ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ে। নইলে তারা রক্ত চুষে মানুষের শরীর ছিবড়ে করে ফেলে দেবে। বিনয় আন্দাজ করে নিল ফল-মিষ্টি, কাপড়-টাপড় জারোয়াদের জন্যই আনা হয়েছে। এসব নিয়েই সুভাষ মজুমদার হিংস্র অরণ্যবাসীদের এলাকায় পা রাখবেন। তার অনুমানটা যে সঠিক সেটা জানা গেল। সুভাষ মজুমদার বললেন, ‘কাকা, আর দেরি করা যাবে না। এবার আমাকে বেরুতে হবে।
তিনি ব্যাগগুলো তুলতে যাবেন, শেখরনাথ বাধা দিলেন–’না না, লা-ডিন ধনপতদের ডাকছি। পেরিমিটার রোড পর্যন্ত তারা ওগুলো নিয়ে যাবে। তোমাকে বইতে হবে না।‘
পেরিমিটার রোড অবধি, কেননা তারপর জেফ্রি পয়েন্টের কারও এমন বুকের পাটা নেই যে জারোয়াদের চৌহদ্দিতে গিয়ে ঢুকতে পারে।
ডাকাডাকি করে লা-ডিনদের আনানো হল। শেখরনাথের নির্দেশে তারা তিনটে ব্যাগ কাঁধে তুলে নিল। এবার সোজা উত্তর দিকে যেতে হবে। সবার আগে আগে শেখরনাথ, বিনয় এবং সুভাষ মজুমদার। তাদের পেছনে পরিতোষ এবং পুনর্বাসনের কর্মীরা।
উদ্বাস্তুরা লম্বা লম্বা ব্যারাকগুলোর এধারে দাঁড়িয়ে চা রুটি-টুটি খাচ্ছিল। শেখরনাথদের, বিশেষ করে সুভাষ মজুমদারকে দেখে তাদের খাওয়া বন্ধ হল। কালই সারা জেফ্রি পয়েন্টের উদ্বাস্তুরা জেনে। গেছে এই চরম দুঃসাহসী, অকুতোভয় মানুষটি তাদেরই জন্য প্রচন্ড বিপদের ভয়কে উড়িয়ে দিয়ে জারোয়াদের বোঝাতে জঙ্গলে যাবেন। খাবার-দাবার ফেলে তারাও দল বেঁধে পিছু পিছু চলল। কারও মুখে টু শব্দটি নেই। আড়াই তিনশো মানুষ নিঃশব্দে পা ফেলছে শুধু। পাহাড় জঙ্গলে ঘেরা বিশাল এই জেফ্রি পয়েন্ট জুড়ে অনন্ত স্তব্ধতা নেমে এসেছে। অথচ আন্দামানের এক কোণে এই দুর্গম ভূখণ্ড অন্য দিন সকাল হতে না-হতেই সরগরম হয়ে ওঠে।
পেরিমিটার রোড অবধি এসে সবাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। উঁচু উঁচু টঙগুলোতে যে বুশ পুলিশরা দিবারাত্রি নজরদারি চালায় তারা পর্যন্ত অবাক বিস্ময়ে সুভাষ মজুমদারকে দেখছে।
লা-ডিনদের কাছ থেকে ব্যাগগুলো নিলেন সুভাষ মজুমদার। কাপড়ের ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিলেন তিনি, আর দুই হাতে অন্য দু’টো ব্যাগ। তারপর সবার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। –’চলি। আপনারা ভয় পাবেন না। আশা করি সব ঠিক হয়ে যাবে।‘
বিনয় মানুষটিকে যত দেখছিল ততই তার বিস্ময় বাড়ছিল। কোথায় তিনি ভয় পাবেন তা নয়, উলটে অগুনতি মানুষকে সাহস দিচ্ছেন।
সুভাষ মজুমদার সামনের দিকে পা বাড়ালেন। বিনয়ের সমস্ত শরীর আমূল কেঁপে গেল। সুভাষ বলেছেন, কার নিকোবর-এ দু’টি জারোয়া ছেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছেন, মিডল আন্দামানের জারোয়াদের মধ্যে গিয়েও কাজ করেছেন। কিন্তু এর আগে কখনও দক্ষিণ আন্দামানের, বিশেষ করে জেফ্রি পয়েন্ট অঞ্চলের জারোয়াদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন নি বা করার সময় পাননি। এখানকার জারোয়ারা হয়তো তাঁকে দেখামাত্র দূর থেকে ঝাঁকে ঝাকে তির ছুঁড়তে থাকবে কিংবা অন্য কোনওভাবে হামলা চালাবে। গভীর অরণ্য থেকে হয়তো কোনও দিনই তাঁর ফেরা হবে না। পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের নিদারুণ সংকট থেকে বাঁচাতে এসে তার প্রাণটাই চলে যাবে কিনা, কে জানে।
কাল বিকেলে এখানে এসেছেন সুভাষ মজুমদার। একটা রাত কাটিয়ে চলে গেলেন উত্তর দিকের জঙ্গলে। কতটুকু সময়ই বা তাঁকে দেখেছে বিনয়। পরার্থে নিজের জীবনকে সঁপে দেবার অজস্র কাহিনি নানা বইয়ে পড়েছে সে; শুনেছে। কিন্তু এই প্রথম একজনকে স্বচক্ষে দেখল, প্রায় নিশ্চিত মৃত্যুকে তুচ্ছ করে মহাবিপজ্জনক এক অভিযানে চলেছেন। উৎকণ্ঠাটা শতগুণ হয়ে বিনয়ের হৃদপিন্ডে যেন চাই চাই পাথরের স্তূপের মতো চেপে বসতে থাকে।
জঙ্গলে ঢুকে গলার স্বর অনেক উঁচুতে তুলে চিৎকার করে কিছু বলতে বলতে সুভাষ মজুমদার এগিয়ে যেতে লাগলেন। এসব ভাষা আগে আর কখনও শোনে নি বিনয়। প্রতিটি শব্দ অত্যন্ত দুর্বোধ্য। ক্রমশ প্রাচীন সব মহাবৃক্ষ এবং ঘন নিবিড় জটিল ঝোঁপঝাড়ের ভেতর দিয়ে সুভাষ মজুমদারের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে গেল। তাঁকেও আর দেখা গেল না।