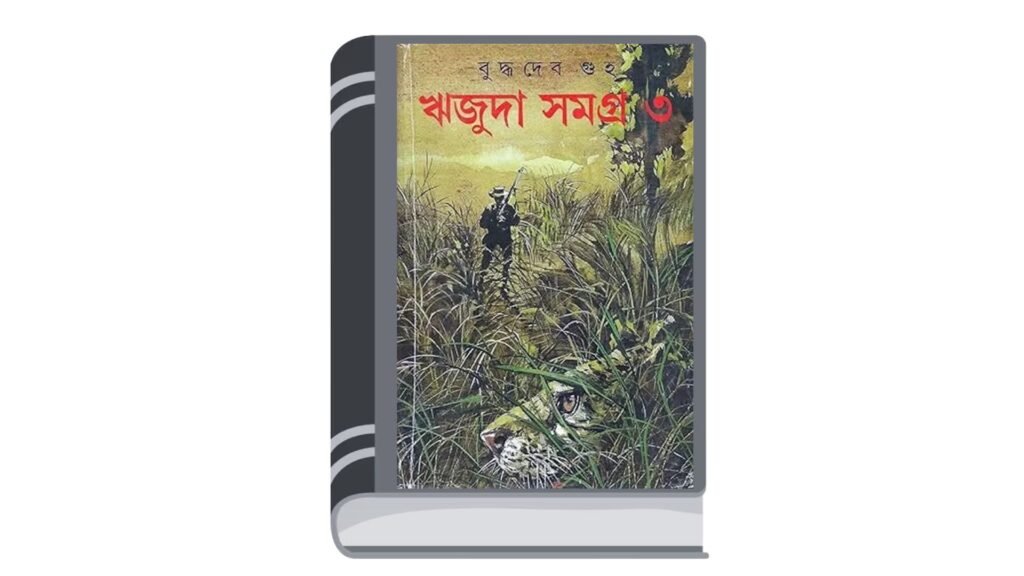ঋজুদার সঙ্গে পুরুণাকোটে
০১.
আমরা ওড়িশার অঙ্গুল ফরেস্ট ডিভিশনের পুরুণাকোটের বন-বাংলোর বারান্দাতে বসেছিলাম। আমরা মানে, ঋজুদা, তিতির আর আমি। ডিসেম্বরের শেষ। হাড়কাঁপানো শীত। রোদটা তেরছাভাবে এসে পড়েছে মাটি থেকে অনেকই উঁচু বারান্দায়। হাতির ভয়ে বড় বড় শালের খুঁটির উপরে মস্ত পাটাতন করে নিয়ে তার উপরে বাংলো বানানো। ঋজুদা সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে একটা মোড়ার উপরে পা দুটি তুলে দিয়ে পরপর তিন কাপ চা খাওয়ার পর গায়ে একটা ফিকে-খয়েরি রঙা পশমিনা শাল জড়িয়ে জম্পেশ করে পাইপ ধরিয়েছে।
তিতির বলল, বাঃ ঋজুকাকা, ফিকে-খয়েরি জমিতে গাঢ় খয়েরি রঙা পাড়টা দারুণ খুলেছে তোমার শালের।
ঋজুদা বলল, শালটা কে দিয়েছিল জানিস?
কী করে জানব? তিতির বলল।
শোনপুরের এই ওড়িশারই এক করদ রাজ্যের মহারাজা সিং দেও সাহেব। এক সময়ে উনি তাঁর রাজ্যের রাজধানী বলাঙ্গীরের একটা মার্ডার-কেস নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। সেই থেকে খুবই বন্ধুত্ব হয়ে যায়। আমাকে বহুবার বলাঙ্গীরে শিকারে যেতেও নেমন্তন্ন করেছিলেন কিন্তু তখন আমার প্রিয় শিকারভূমি ছিল কালাহান্ডি।
কালাহান্ডি! কী অদ্ভুত নাম রে বাবা। কালোহাঁড়ি?
ইয়েস। ওড়িশার কালাহান্ডি এক আশ্চর্য সুন্দর করদ রাজ্য ছিল। সুন্দর কিন্তু ভয়াবহ। অমন নৈসর্গিক দৃশ্য ভারতের কম জায়গাতেই আছে। মানে, বলতে চাইছি আলাদা রকম। বড় বড় কাছিমপেঠা, ন্যাড়া, বাদামি-রঙা পাহাড়গুলো, মনে হয়, অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক জন্তুরই মতো শুয়ে আছে।
যখন পুব-আফ্রিকাতে প্রথমবার যাই তখন সেখানকার কোনও কোনও জায়গা দেখে কালাহান্ডির কথা আমার বারবারই মনে পড়েছিল।
কী শিকার করতে যেতে কালাহান্ডিতে?
আমি বললাম।
বাঘ। আবার কী! যদিও অন্য শিকার, বিশেষ করে বড় বড় ভালুক, বুকে সাদা ‘V’ চিহ্ন আঁকা, অনেকই ছিল। SLOTH BEAR ছাড়াও। সুন্দরবনের সব বাঘই যেমন মানুষখেকো (পশ্চিমবঙ্গের বনবিভাগ যাই বলুন না কেন), কালাহান্ডির সব বাঘও মানুষখেকো ছিল। অন্তত আমি যে সময়ের কথা বলছি, আজ থেকে বছর পঁয়ত্রিশ আগের কথা, সেই সময়ে ছিল।
তিতির বলল, তুমি তো তখন ছেলেমানুষ ছিলে।
আমি এখনও ছেলেমানুষ। তোর মা অন্তত তাই বলেন।
কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, মানুষের সংখ্যা আমাদের দেশে এমনই বেড়েছে ও বাড়ছে যে, গিনিপিগ বা শুয়োরেরাও লজ্জা পাবে। এখন মানুষই সর্ব-খেকো হয়ে গিয়ে অন্য সব প্রাণীদের হয় বংশ নাশ করছে নয়তো তাড়িয়ে দিয়েছে তাদের পুরনো বাসভুমি থেকে সেসব জায়গাতে, যেখানে এখনও কিছু গভীর জঙ্গল বেঁচে আছে।
তিতির কী একটা বলতে যাচ্ছিল এমন সময়ে একটা কালো অস্টিন গাড়ি এসে দাঁড়াল পুরুণাকোট বন বাংলোরই সামনে। গাড়িটা জঙ্গলের দিক থেকে এল।
ঋজুদা বলল, অস্টিন। এই গাড়িগুলোই লন্ডন শহরের ট্যাক্সি। লন্ডন-এর ট্যাক্সি হিসেবে অন্য কোনও গাড়ি দেখাই যায় না। ট্যাক্সি বলতে শুধু ইংলিশ গাড়ি। অস্টিন, কালো-রঙা।
ঋজুদার কথা শেষ হওয়ার আগেই সে গাড়ির পিছনের দরজা খুলে এক ছোট্টখাট্ট ভদ্রলোক নামলেন। ধুতি ও শিয়ালেরঙা সার্জ-এর গরম পাঞ্জাবি পরা তার উপরে কালো রঙা জওহর কোট। ফ্লানেলের। গাড়ি থেকে নেমেই উপরের দিকে মুখ করে ঋজুদাকে জোড়হাতে নমস্কার করে বললেন, প্রণাম আইজ্ঞাঁ।
ঋজুদা সম্ভবত গাড়ি থেকে নামার সময়ে ভদ্রলোককে চিনতে পারেনি কিন্তু। গলার স্বর শুনে চিনতে পেরেই রেলিং-ঘেরা বারান্দার রেলিং-এর সামনে এসে করজোড়ে নমস্কার করে বলল, হোয়াট আ প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ! নমস্কার পট্টনায়েকবাবু। আপনি কেমিতি জানিলানি যে, মু এটি আসিচি? আসন্তু আসন্তু।
পট্টনায়েকবাবু হেসে বললেন, আইজ্ঞা আপনংকুতে আগমন নাহি, সে তো আবির্ভাব হেদা। সব্বেমানে জানিচি।
ঋজুদা জোরে হেসে উঠল।
পট্টনায়েকবাবু ছোট ছোট পা ফেলে সিঁড়ি বেয়ে খুটখুট করে দোতলাতে উঠে এসে বললেন, এই সাত সকালেই কেন এলাম তা নিশ্চয়ই ভাবছেন আপনি।
তা তো ভাবছিই! কিন্তু কোথা থেকে এলেন এখন?
ঢেনকানল থেকে, অঙ্গুল হয়ে। অঙ্গুলেও থাকতে হয়। ঢেনকানলেও কাজ হচ্ছে আমার। তাই অন্ধকার থাকতে থাকতেই বেরিয়ে পড়লাম, আপনি কোথাও বেরোবার আগেই যাতে আপনাকে ধরতে পারি।
তিতির ভিতর থেকে একটা কাপ নিয়ে এসে চা ঢেলে দিল পট্টনায়েকবাবুকে। বিস্কিটের প্লেট এগিয়ে দিল। তারপর বলল, চিনি ক’ চামচ?
না না, চিনি দেবেন না, দুধও নয়। আমি ডায়াবেটিক। আর দুধ খেলেও অম্বল হয়, বয়স তো হল।
পরিষ্কার বাংলাতে বললেন তিনি।
আমাদের অবাক হতে দেখে ঋজুদা বলল, অধিকাংশ শিক্ষিত ওড়িয়াই বাংলা শুধু বলতেই পারেন না, পড়তেও পারেন। অথচ শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে সম্ভবত হাজারে একজন ওড়িয়া বলতে পারেন বা পড়তে পারেন। এমনি কি আর আমি বাঙালিকে কূপমণ্ডুক বলি! পশ্চিমবঙ্গের নেতা থেকে সেক্রেটারি, সেক্রেটারি থেকে কেরানি সকলেই কূপমণ্ডুক।
পট্টানায়েকবাবু একটা মুচকি হেসে বললেন, তা ছাড়াও একটা ব্যাপার আছে।
কী ব্যাপার?
বাঙালিরা প্রায় সকলেই এক দুরারোগ্য সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স-এ ভোগেন, সুপিরিয়রিটির কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান না করেই।
কথাটা শুনে আমাদের কারুরই ভাল লাগল না। কারণ, আমরা বাঙালি।
ঋজুদা একটু চুপ করে থেকে বলল, কথাটা আমাদের শুনতে খারাপ লাগলেও কথাটা হয়তো সত্যিই। ওতে বাঙালির ভালর চেয়ে খারাপই হয়েছে অনেক বেশি।
তারপর বলল, এবারে বলুন, ভোর রাতে এই শীতের মধ্যে বেরিয়ে এখানে আসা হল কেন?
গরজ বড় বালাই ঋজুবাবু। আপনি তো বাঘমুণ্ডাতে বহুবার গিয়ে থেকেছেন।
তা থেকেছি। বাঘঘমুণ্ডা খুবই প্রিয় জায়গা ছিল আমার। যখন এদিকে আসতাম নিয়মিত বছর পঁচিশ-তিরিশ আগেও। এবারে এসেছি আমার এই দুই সাগরেদ, রুদ্র আর তিতিরকে ‘সাতকোশীয়া গন্ড’ ঘুরিয়ে দেখাব বলে। শুনতে পাচ্ছি নাকি। দু-এক বছরের মধ্যেই এই অঞ্চল অভয়ারণ্য হিসাবে ঘোষিত হবে।
হুঁ। অভয়ারণ্য! মানুষের জন্যও অভয় দিতে বলুন। মানুষও বড় ভয়ে ভয়ে আছে।
তারপর বললেন, আপনার কি একছেলে এক মেয়ে? এরাই? আর নেই?
ওঁর কথাতে ঋজুদাতো বটেই, আমরাও হো হো করে হেসে উঠলাম।
পট্টনায়েকবাবু অপ্রতিভ হলেন।
হাসির দমক কমলে, ঋজুদা বলল, কোনও মেয়ে আমাকে বিয়েই করল না মশাই তার ছেলে-মেয়ে আসবে কোথা থেকে?
তবে? এরা?
এরা আমার কমরেডস। এদের দেখে ভাববেন না এরা সাধারণ বাঙালি এবং খোকা-খুকু। এরা আমার সঙ্গে আফ্রিকাতে, সেশেলস-এ এবং ভারতের বহু। জায়গায় গেছে এবং বন্দুক-রাইফেল চালাতে এবং বুদ্ধিতেও এরা আমাকেও সহজেই হার মানায়।
তিতির বলল, আমি তো সেশেলস-এ যাইনি। তা ছাড়া এটা বাড়াবাড়ি হচ্ছে ঋজুকাকা। বিনয় ভাল, কিন্তু অতিরিক্ত বিনয় নয়। সেটা বরং লক্ষণ হিসাবে খারাপই।
পট্টনায়েকবাবু বললেন, তবে তো চমৎকার। আমি যে কাজে এসেছি সে কাজ আরও সহজ হবে।
এখন বলুন কাজটা কী?
বাঘমুণ্ডাতেও আমার কাজ চলেছে। অঙ্গুলের নিলামে এবারে ঢেনকানলের অনেকগুলো ব্লক এবং বাঘমুণ্ডার ব্লকও ডেকেছিলাম। ভাল কাঠ আছে বাঘঘমুণ্ডাতে সে কথা তো আপনি জানেনই। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসে সিজন খোলার পরে মার্কা মারা শেষ হতে না হতে এক আপদ এসে উপস্থিত হল। বাঘঘমুণ্ডাতে হাতিরই যা বিপদ ছিল। তাও দিনে তত নয়। কিন্তু এবারে সিজন খোলার পর অক্টোবর থেকে নভেম্বর অবধি আমার ন’জন কাবাড়িকে খেয়ে ফেলল এক মানুষখেকো বাঘে। তারা সবাই আবার করতপটা গ্রামের মানুষ। অঙ্গুল থেকে দিনমানে আমার এখানে আসার উপায়ই নেই। কারণ, আপনি তো জানেনই, আসতে গেলে করতপটার উপর দিয়েই আসতে হয়। তাইতো অন্ধকারে এলাম। ফিরতেও হবে অন্ধকারেই।
তারপর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ডিসেম্বরের গোড়াতে সব কাবাড়িরাই কাজ বন্ধ করে ফিরে গেল। প্রত্যেক পরিবারকে মোটা ক্ষতিপূরণও দিলাম। কিন্তু জীবনের ঘাটতির ক্ষতি কি পয়সা দিয়ে কোনওদিনও পূরণ করা যায়? বিবেকেও লাগে। আমি ঠিকাদার, পয়সা রোজগারের জন্য ঠিকাদারি করি আর আমার হয়ে কাজ করতে এসে এই ন’জন গরিব মানুষ প্রাণ দিল মানুষখেকোর মুখে। তাই অঙ্গুলের ফরেস্ট অফিস থেকে আপনি আসছেন খবর পাওয়া মাত্রই ঠিক করে রেখেছিলাম যে, যেদিন এসে পৌঁছোবেন বিকেলে বা রাতে, তার পরদিনই ভোরে আপনাকে এসে ধরব।
ডিসেম্বরে বাঘটা কোনও মানুষ ধরেনি?
ঋজুদা জিজ্ঞেস করল।
আমার সব লোক এবং করতপাটার সব কাবাডিরা সদলে চলে গেল নভেম্বরের ত্রিশ তারিখের মধ্যেই। তার ধরবে কাকে?
তারপরেই বললেন, তবে ধরেনি, তা নয়। ধরেছে, পুরুণাকোটেরই এক ভিখারিনী বাইয়ানীকে আর টুকা আর পুরুণাকোটেরই মাঝে যে ছোট্ট গ্রামটা আছে, নাম ভুলে যাচ্ছি, সেই গ্রামের একটা ছেলেকে।
তিতির বলে উঠল, বাইয়ানী মানে কী?
ঋজুদা বলল, ওড়িয়াতে পাগলিনীকে বাইয়ানী বলে।
অন্য জায়গাতেও তো মানুষ ধরেছে। তা হলে বাঘটার নাম বাঘঘমুণ্ডার বাঘ। হল কেন?
ঋজুদা জিজ্ঞেস করল, পট্টনায়েকবাবুকে।
উনি বললেন, অন্য জায়গাতে বিশেষ যায় না, বাঘমুণ্ডা গ্রামের কাছাকাছিই ঘোরে-ফেরে। বাঘটার হেডকোয়ার্টাস হচ্ছে বাঘঘমুণ্ডার হাতিগির্জা পাহাড়ে।
হাতিগির্জা পাহাড়!
তিতির বেশ জোরেই চেঁচিয়ে উঠল। বলল, ‘পর্ণমোচী’ পত্রোপন্যাসে পড়েছি হাতিগির্জা পাহাড়ের কথা।
আমি বললাম, এখানের হাতিরা বুঝি খ্রিস্টান? গির্জাতে গিয়ে উপাসনা করে?
সকলেই হেসে উঠল আমার কথাতে।
তিতির বলল, বাঘঘমুণ্ডার কথাও পড়েছি আমি নগ্ন নির্জন’ উপন্যাসে।
পট্টনায়েকবাবু চায়ের কাপটা সশব্দে ডিশ-এর উপরে নামিয়ে রেখে একটু অধের্য গলায় বললেন, তা হলে কী হল আমার আর্জির ঋজুবাবু? আমাকে কি ফেরাবেন আপনি?
ঋজুদা একটু চুপ করে থেকে বলল, এদের নিয়ে একটু ঘুরতে এসেছি। তবে, মানুষখেকো বাঘটা আমরা থাকতে থাকতে যদি কোনও মানুষ মারে তা হলে একটা চেষ্টা করা যেতেই পারে অবশ্য। আপনি যখন এমনভাবে দৌড়ে এসেছেন।
মানুষ না মেরে যদি গোরু-টোরু মারে?
গোরু-টোরুও মারে নাকি? তবে তো বাঘটা বেশ বহাল তবিয়তেই আছে বলতে হবে। যে সব বাঘ বুড়ো, বা যে-কোনও কারণেই হোক অশক্ত হয়ে যায়, তারাই সাধারণত মানুষ ধরে। মানুষ তো বাঘের স্বাভাবিক খাদ্য নয়। গোরুও অবশ্য নয়।
তা জানি না, কিন্তু এই বাঘটার তো দেখি বাছ-বিচার নেই। চেহারাতেও সে দশাসই। বাঘঘমুণ্ডার বন-বাংলোর পিছনের মাঠ থেকে একটা নধর গোরু ধরে সেটাকে হাতিগির্জা পাহাড় অবধি কিছুটা পিঠে তুলে, কিছুটা টেনে, কিছুটা হেঁচড়ে নিয়ে গিয়ে খেয়েছিল। তা হলে কতখানি শক্তি ধরে বুঝতেই পারছেন।
তাই? তা হলে যদি কোনও kill হয়, আমাকে খবর দেবেন। চেষ্টা করে দেখব। আমরা কিন্তু এই অঞ্চলে ঠিক সাতদিনই আছি। ফেরার রিজার্ভেশনও করা আছে। কটক থেকে। ফিরতেই হবে। তারই মধ্যে এদের দু’জনকে মহানদীর এপার-ওপারের সব জঙ্গল দেখাতে হবে, অতএব বুঝতেই পারছেন! তবে যেখানেই যাই, রাতে ফিরে এসে পুরুণাকোটেই থাকব। এখানেই খবর পাঠাতে বলবেন। রাতে kill হলে যেন ভোরেই এসে খবর দেয়। এবং এমন লোককেই খবর দিতে পাঠাবেন যে, সে-ই যেন আমাদের kill-এর জায়গাতে নিয়ে যেতে পারে।
হ্যাঁ। হ্যাঁ। তাতো বটেই।
কিন্তু মানুষখেকো বাঘ শিকার তো আর তা বলে তুড়ি মেরে করতে পারব না। মানুষ-মারা পিস্তল ছাড়া তো সঙ্গে কিছুই আনিনি এবারে। মানে, অন্য কোনও আগ্নেয়াস্ত্র।
ঋজুদা বলল, পট্টনায়েকবাবুকে।
আরে সেজন্য চিন্তা নেই। ঢেনকানল-এর ছোট রাজকুমার, মানে, নিনি কুমারের বাড়ি থেকে নিয়ে আসব।
ও। নিনি কুমারের কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম। তিনি তো আমার চেয়ে অনেকই ভাল শিকারি। তাঁকে এই বাঘ মারতে বলেননি কেন?
আরে তিনি থাকলে তো এখানে! চার মাসের জন্য ইউরোপে গেছেন। ফিরবেন জানুয়ারির শেষে।
তা তিনি না থাকলে বন্দুক-রাইফেলই বা পাবেন কী করে?
সে আমার দায়িত্ব। তা ছাড়া ঢেনকানল-এর রাজবাড়ি ছাড়াও আমার অন্য অনেক বন্ধু আছে।
পরের ওয়েপন দিয়ে এররকম বিপজ্জনক শিকার কখনও করিনি! করা বিপজ্জনকও বটে।
ঋজুদা চিন্তিত মুখে বলল।
একবার না হয় আমাকে ধনে-প্রাণে বাঁচাতে একটু বিপদের ঝুঁকি নিলেনই ঋজুবাবু। তা ছাড়া, আপনার কোনও বিপদ হবে না। আপনি ঋদ্ধিমান পুরুষ।
বিপদের কথা কি কেউ বলতে পারে পট্টনায়েকবাবু? কার যম যে পিছনে কখন এসে দাঁড়ায়, সে কথা মানুষ যদি জানত!
তারপর কী একটু ভেবে ঋজুদা বলল, ঠিক আছে। কথা দিলাম আপনাকে for old times sake!
পট্টনায়েক বাবু চেয়ার ছেড়ে ওঠার সময় বললেন, বাবাঃ। সাতটা বেজে গেল। কত জায়গাতে যেতে হবে। কত কাজ! কিন্তু নিশ্চিত হয়ে যাচ্ছি। এবারে একটা সুরাহা হলেও হতে পারে।
.
অনেক গল্প-টল্পর পর এক এক করে চান সেরে ব্রেকফাস্ট খেয়ে অঙ্গুলের বিমলবাবু, শ্রীবিমলকৃষ্ণ ঘোষ, যে জিপটা আমাদের ব্যবহারের জন্য দিয়েছিলেন, সেটা নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম টিকরপাড়ার দিকে। আমিই জিপ চালাচ্ছিলাম। মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রার জিপ। এখন প্রায় সাড়ে দশটা বাজে।
ঋজুদা বাঁদিকের সিটে বসে পাইপ ধরাতে ধরাতে বলল, জিপে বসে পাইপ খাওয়ার এই অসুবিধা। চারদিক থেকে হাওয়া ঢুকতে থাকে। পইিপ ধরানোতে মহা হাঙ্গামা। যদিও বা ধরল, তো নিভে যায় পরক্ষণেই। ধৈর্যের পরীক্ষা!
আমি একটু আস্তে করলাম গতি। তিতির পিছন থেকে ফুট কাটল, পাইপ খাওয়াটা তো ছেড়ে দিলেই পার। পাইপ খেলে জিভে ক্যানসার হয় তা বুঝি তুমি জানো না?
জানব না কেন? তবে পাইপ তো তিরিশ বছর ধরে খাচ্ছি। ভাত না খেলেও চলে, পাইপ না খেলে চলে না। আমাদের বাড়ির উলটো দিকের বাড়ির যোগেনবাবু পান-তামাক-মদ কিছুই খেতেন না। একেবারে সদাচারী, সদালাপী, অজাতশত্ৰু মানুষ। মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে জিভের ক্যানসারে মারা গেলেন। কীসে যে কী হয়, তা আল্লাই জানেন!
পথটা গেছে সোজা আর তার ডানদিক দিয়ে একটা উপল-বিছানো পাহাড়ি নদী চলেছে ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ঘন বনের ভেঁড়া-ঘেঁড়া চন্দ্রাতপের নীচে নীচে রোদ আর ছায়ার সঙ্গে খেলা করতে করতে। নদীর মাঝে মাঝে অনেকগুলো ছোট ছোট প্রপাতের সৃষ্টি হয়েছে। চলকে-যাওয়া নুপূর-পরা জল ঝিলমিল করে উঠছে শীত সকালের রোদ গায়ে পড়াতে। একটা বাদামি কালো কুম্ভাটুয়া পাখি ডাকছে। নদীর ওপার থেকে, গুব-গুব-গুব-গুব করে। শীতের হাওয়াতে নলি আর কণ্টা বাঁশের বনে কটকটি আওয়াজ উঠছে। বাঁশের গায়ের হালকা পাতলা হলুদ আর পেঁয়াজখসি-রঙা খোলস উড়ে উড়ে পড়ছে পথের উপর আলতো হয়ে।
নদীতে কত্ত রকমের যে পাথর! এরকম নদী দেখলেই আমার ইচ্ছে করে চড়ুইভাতি করতে বসে যাই।
তিতির বলল।
যা বলেছ!
আমি বললাম।
এই নদীর, নদী নয়, একে স্থানীয় মানুষরা নালা বলে, নাম বোষ্টম নালা। পুরুণাকোটের আগে বাঁক নিয়ে চলে গেছে বাঁয়ে বাঘমুণ্ডার দিকে। সেখানে আবার এর নাম নন্দিনী।
বাঃ। ভারী সুন্দর নাম তো। এই নালাদের কথাও পড়েছি ‘জঙ্গলের জার্নাল’-এ।
তারপরে একটু চুপ করে, থেমে ঋজুদা বলল, আমরা মহানদী পেরোব ফেরি-নৌকোতে। গাড়ি, বাস, ট্রাক, সবই ফেরি করেই পেরোয়। যে মহানদী দেখবি, তাই ওড়িশার মুখ্য নদী। আমাদের যেমন গঙ্গা। আসামের যেমন ব্রহ্মপুত্র।
‘সাতকোশীয়া গন্ড’ শব্দ দুটির মানে কী ঋজুকাকা?
তিতির বলল।
‘গন্ড’ মানে ওড়িয়াতে গিরিখাত বা Gorge। আর ‘কোশ’ মানে হচ্ছে ক্রোশ। ‘সাতকোশীয়া’ মানে হল সাত ক্রোশ অর্থাৎ চোদ্দো মাইল। কিলোমিটারের হিসাব তো এই সেদিন হল।
মহানদীর উৎস যদিও অনেক দূরে, এখানে মহানদী দুপাশের ঘন জঙ্গলাবৃত উঁচু পাহাড়ের মধ্যের গিরিখাত দিয়ে বয়ে গেছে চোদ্দো মাইল। গন্ড শেষ হয়েছে বডোমূল-এ গিয়ে। বিনকেই থেকে বড়োমূল। তারপর মহানদী চওড়া হয়ে ছড়িয়ে গেছে। এই নদী বেয়েই লক্ষ লক্ষ বাঁশ বেঁধে এক একটি ভেলা বানানো হত। তারই উপর ভেলার জিম্মাদারদের রান্না-বান্না, খাওয়া-দাওয়া, গানবাজনা, লণ্ঠন জ্বেলে রাতে তাস খেলা। গোরু-বাছুরও উঠত তাতে কখনও সখনও। পেট্রল লাগত না, দাঁড় লাগত না, কোনও তাড়াই ছিল না। নদী যখন যেমন গতিতে ভাসিয়ে নিয়ে যেত, কখনও ধীরে, কখনও জোরে, তেমনই যেত তারা। চোদ্দো মাইল যেতেই দু থেকে তিন দিন লাগত।
লাগত কেন? এখন লাগে না?
এখন কাগজ তো আর কাঠের মণ্ড বা বাঁশ থেকে তৈরি হয় না। পরিবেশ বাঁচাতে এখন রি-সাইক্লিং করেই কাগজ তৈরি হয়। আরও নানা উপায়ে বানানো হয়ও এবং হবে ভবিষ্যতে।
তবে তো জঙ্গল অনেক বাড়বে।
আমি বললাম।
বাড়ছে আর কোথায় বল? সরষের মধ্যেই যে ভূত ঢুকে গেছে। আমরা মানুষরাই রাহুগ্রস্ত হয়ে গেছি, আমাদের লোভেই চুরি করে বন নষ্ট করছি। এত মানুষ যদি কোনও দেশে থাকে এবং তাদের সংখ্যা যদি রোজই বাড়তে থাকে, জন্মহার যদি কমানো না যায় তবে পরিবেশ কেন, বন্যপ্রাণী কেন, কোনওকিছুই বাঁচবে না। সবই বুভুক্ষু আর লোভীদের হাতে নষ্ট হয়ে যাবে। অবধারিতভাবে নষ্ট হবে। আমাদের কেতাবি অর্থনীতিবিদরা যাই বলুন না কেন, তাঁরা যেহেতু নিজের দেশকে তেমন করে চেনেন না, জানেন না, তাঁদের বই-পড়া বিদ্যেতে এ দেশের প্রকৃত কোনও উন্নতিই হবে না।
আমরা চুপ করেই রইলাম। বারেবারেই আমরা বুঝতে পারি ঋজুদা আমাদের দেশকে কতখানি ভালবাসে। অথচ সে ইচ্ছা করলে মহাসাহেব হতে পারত। পৃথিবীর কোন দেশে যে যায়নি! আমাদেরও তো সঙ্গে করে নিয়ে গেছে কত দেশে। আর স্বদেশের কথা তো ছেড়েই দিলাম। এ দেশকে এত ভালভাবে কম মানুষই জেনেছেন।
বিদেশে গেলেই দেশে ফিরে লোকে আমাদের দেশকে তাচ্ছিল্যর চোখে দেখে, ঠোঁট বেঁকায়। একমাত্র ঋজুদাকেই দেখলাম, সারা পৃথিবী বহুবার ঘুরেও যে বলে আমার দেশের মতো দেশ হয় না, এ দেশের গ্রামীণ মানুষদের মতো মানুষ হয় না।’ তিতির, আমার আর ভটকাই-এর মধ্যে অজানিতেই এক গভীর দেশাত্ববোধ জন্মেছে ঋজুদার সংস্পর্শে এসেই।
তিতির হঠাৎ বলল, ভটকাইটা এবারে খুব মিস করবে। সাতকোশীয়া গন্ড ওর দেখা হল না।
মায়ের অসুখে যদি সেবাই না করল, তা হলে সে ছেলের সব গুণ জলে গেল। এখন তো ওর বেড়াতে আসার কথা নয়। ছেলেটার অনেক গুণ কিন্তু এইসব শিক্ষা তাকে দেওয়া হয়নি সম্ভবত। স্কুলে বা কলেজে ভাল রেজাল্ট করা, বড় চাকরি করা বা ব্যবসা করা, এসবের কোনওই দাম নেই আমার কাছে, যদি কোনও মানুষের কর্তব্যজ্ঞান না থাকে, বিবেক না থাকে। ও কী করে যে মায়ের এমন অসুখ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের সঙ্গে আসতে চাইছিল তাই ভেবে পাইনা।
আর কতক্ষণ লাগবে ঋজুদা? টিকরপাড়া পৌঁছোতে?
আমি বললাম।
ধর, আর মিনিট পনেরো। খুব বেশি হলে। দেখছিস না জঙ্গল কেমন ফিকে হয়ে এল, আগে পথের পাশে দু-একটা তৈলা দেখা যাচ্ছিল। আর এখন তো দুধারেই চষা মাঠ।
তৈলা মানে কী?
তৈলা একটা ওড়িয়া শব্দ। ঘন জঙ্গলের মধ্যে জঙ্গল পরিষ্কার করে যেখানে চাষাবাদ করা হয়, তাকে বলে তৈলা। মানে, সেই জায়গাটাকে। জঙ্গলের খামার আর কী!
এমন সময়ে রিয়ার-ভিউ মিরারে দেখলাম পিছন থেকে একটা মোটর সাইকেল ঝড়ের মতো আসছে ধুলো উড়িয়ে, বিপজ্জনক এবং অবিশ্বাস্য গতিতে। মোটর সাইকেল তো না, যেন মনো-এঞ্জিন প্লেন নিয়ে ট্যাক্সিইং করছে। আমি জিপ বাঁয়ে করলাম যাতে তার অসুবিধে না হয় আমাদের পেরিয়ে যেতে। ততক্ষণে সে এসে পৌঁছোলো আমাদের পাশে। কিন্তু ওভারটেক না করে বাঁ হাত দিয়ে আমাকে জিপ থামাতে ইশারা করল, করেই জিপের সামনে উঠে এল পথে।
কীরে! আমাদের পাইলটিং করে নিয়ে যেতে পাঠাল না কি কেউ একে? ব্যাপারটা কী?
ঋজুদা বলল।
তিতির বলল, ডাকাত-টাকাত নয় তো?
ঋজুদা বলল, সুন্দরী তুই ছাড়া আমাদের কাছে নিয়ে পালাবার মতো তো আর কিছুই নেই। তোকেই বোধহয় নিতে এসেছে।
ততক্ষণে মোটর সাইকেলের গতি কমে এসেছে। সে যেহেতু রাস্তার মাঝখানে আছে আমারও গতি কমাতে হল জিপের। গতি একেবারেই কমে এল মোটর সাইকেলের। দেখলাম, ঋজুদা কোমরের বেল্ট-এর সঙ্গে বাঁধা পিস্তলের হোলস্টারের বোতামটা পুটুস করে খুলল।
লোকটা মোটর সাইকেলটাকে দাঁড় করিয়ে জিপের বাঁদিকে ঋজুদার কাছে এসে বলল, কাম্ব সারিলা স্যর।
হেল্বা কেন?
ঋজুদা জিজ্ঞেস করল।
সেই বাঘাঘটা পট্টনায়েকবাবুর ছেলেটাকে ধরে নিয়ে গেল।
সে কী? কোথায় ছিল সে? মরে গেছে?
মরবে না? বড় বাঘে যাকে ধরে, সে কি আর বাঁচে স্যার!
তাকে মেরে বনের মধ্যে টেনে নিয়ে গেছে।
কোথায় ধরল?
বোস্টম নালার পাশে একটা বড়ো কুচিলা গাছ আছে না? সেই গাছের তলাতে ধরেছে। এখন আর কথা বলে সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না স্যর। তাড়াতাড়ি আসুন আপনি। সেই পট্টনায়েক বুড়োটা হার্টফেল করে এতক্ষণে মরেই গেল না কি, কে জানে!
বলেই, মোটর সাইকেল ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, মু পলাইলি। আপনি দয়া করিকি চঞ্চল আসন্তু।
ঋজুদা আমাকে বলল, ঘোরা জিপ। সবই তোদের কপাল। কথায় বলে না, চেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে। মনে আছে রুদ্র, হাজারিবাগের মুলিমালোঁয়ায় খুনের পরে খুন, না ভেনেও বা উপায় ছিল কী?
মনে আবার নেই!
আমি বললাম।
‘অ্যালবিনো’ বইটা কিন্তু তুমি দারুণ লিখেছিলে রুদ্র। আমার বড়মামা পর্যন্ত উচ্ছ্বসিত। যিনি বলেন, বাংলা ভাষায় সব ম্যাদামারা সাহিত্য হয়। বাংলা বই ছুঁয়ে পর্যন্ত দেখেন না। সেই তিনিই স্বয়ং প্রশংসার ঝড় বইয়ে দিলেন। আনন্দ পাবলিশার্স-এর বই, না?
তিতির বলল।
হ্যাঁ। ঋজুদা সমগ্রতে আছে।
আমি বললাম, জিপ ঘোরাতে ঘোরাতে। পুরুণাকোটে পৌঁছে দেখলাম, বনবাংলোর সামনেটাতে একটা ছোটখাটো জটলা মতো হয়েছে। গাড়ির পিছনের দরজা খুলে পট্টনায়েকবাবু বিভ্রান্ত হয়ে বসে আছেন। দুটো শটগান নিয়ে দুজন লোক সেই জটলার মধ্যে আছে। আরও একজন আসছে দেখলাম একটা একনলা গাদা বন্দুক নিয়ে।
আমরা যেতেই সকলে একসঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করল, বিভিন্ন স্বরগ্রামে। তখন মোটরসাইকেল চালিয়ে-আসা লোকটা তাদের ধমক দিয়ে বলল পট্টি করুনান্তি। সব্বে চুপ যাউ।
ঘটনাটা জানা গেল। পট্টনায়েকবাবু যখন আমাদের কাছে এসেছিলেন বাংলোয়, তখন তার বড় ছেলে যুধিষ্ঠির ড্রাইভিং-সিটেই বসেছিল। সে-ই নাকি গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এসেছিল ঢেনকানল থেকে। যদিও ড্রাইভারও ছিল। আমরা তাকেই ভেবেছিলাম ড্রাইভার। যুধিষ্ঠির খুবই লাজুক প্রকৃতির ছেলে ছিল। পট্টনায়েকবাবু বলা সত্ত্বেও সে নামতে চায়নি গাড়ি থেকে। তার বিয়েও নাকি ঠিক করে ফেলেছিলেন পট্টনায়েকবাবু।
বাংলো থেকে নেমেই ওঁরা গাড়ি করে জঙ্গলে গিয়েছিলেন। জঙ্গলে বিপুল পরিমাণ গাছ, কাটা অবস্থায় পড়ে ছিল, যা মোষ দিয়ে জঙ্গল থেকে ঢোলাই করে এনে পথপাশের কোনও উঁচু জায়গাতে সাজিয়ে রেখে ট্রাক-এ লোড করার কথা ছিল। কাবাড়িরা তো পালিয়েইছে, অতজন মানুষকে বাঘে নেওয়ার পর থেকে কোনও লোক মোষ নিয়ে ঢোলাই করতেও যেতে চায়নি। ট্রাক ড্রাইভার এবং খালাসিরাও না। দামি, কাটা গাছের বল্লাগুলো কেউ চুরি-টুরি করছে কি না তাই সরেজমিনে তদন্ত করতেই গাড়ি করে পট্টনায়েকবাবু, তাঁর ছেলে যুধিষ্ঠির এবং তাঁদের মুহুরি মহান্তিবাবু জঙ্গলে গিয়েছিলেন। তাঁরা গাড়ি থেকে নামবেন নাই ঠিক করেছিলেন। আস্তে আস্তে গাড়ি চালিয়ে তাঁরা পুরো জঙ্গলটা ঘুরে রাস্তা থেকেই যতটা দেখা এবং অনুমান করা যায় তা দেখে এবং করে ফিরে আসছিলেন।
মহান্তিবাবুর তত্ত্বাবধানেই গাছ সব কাটা হয়েছিল। জঙ্গলের গভীরে নন্দিনী নালার পাশে তাঁদের বাঘমুণ্ডার ক্যাম্প ছিল। নামেই ক্যাম্প কিন্তু তাঁবু নেই। বাঁশ বেড়ার গায়ে মাটি লেপা এবং উপরে ঘাসের ছাউনি দেওয়া তিনখানি ঘর। একখানি ছিল মহান্তিবাবুর। তাতে একটা কাঠের পাটাতনের খাট আর হিসাবপত্র করার কাগজ-টাগজ থাকত। অন্য দুটো ঘরে কাবাড়িরা খড় পেতে মাটিতে শুত ঘরের মধ্যে আগুন করে। বাইরে মাটির হাঁড়িতে রান্না করত। এখন সে সব ঘর হাট করে খোলা পড়ে আছে। জঙ্গল দেখে এসে ওঁরা যখন ক্যাম্পের কাছে পৌঁছোন তখন মহান্তিবাবু বলেন, বাঘমুণ্ডা ছেড়ে তড়িঘড়ি পালিয়ে যাওয়ার সময়ে তাঁর গড়গড়াটা ঘরে ফেলে এসেছেন। এক দৌড়ে ঘরে ঢুকে সেটা নিয়ে আসবেন। কাগজপত্র সব আগেই সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন।
ঝকঝক করছে রোদ্দুর জঙ্গলময়। ডিসেম্বরের সুনীল আকাশ। এই দিনমানে কোনওরকম ভয়কে প্রশ্রয় দিতেও লজ্জা করে। তা ছাড়া, বাঘ তো আর ওঁদের ক্যাম্পের ঘরে ঢুকে মহান্তিবাবুর খাটে শুয়ে থাকবে না।
ক্যাম্পের সামনে ও পিছনে এবং পাশেও আগাছা পরিষ্কার করা ছিল। হরজাই ও জ্বালানি কাঠের গাছও কেটে ফেলায় ফাঁকা ছিল এলাকাটুকু। ওখানেই মুহুরি আর কাবাড়িদের, ঢোলাইওয়ালাদেরও ওঠা-বসা রাতে আগুন করে আগুন পোয়ানো, সকালে ও রাতে রান্নাবান্না। পাশ দিয়েই বয়ে গেছে নন্দিনী নালা। জলের সুবিধে দেখেই ওখানে ক্যাম্প করা হয়েছিল।
মহান্তিবাবু বললেন, আপনারা গাড়িতেই বসুন, আমি যাব আর আসব। রাস্তা থেকে ক্যাম্পটি দেখাও যাচ্ছিল।
মহান্তিবাবু নেমে গেলে যুধিষ্ঠির বলল, বড় হিসি পেয়েছে, বাবা, মহান্তিবাবু ফিরে আসতে আসতে আমি নেমে হিসি করে নিই।
ক্যাম্পটা, হাতিগির্জা পাহাড়ের দিক থেকে এলে পথের ডানদিকে পড়ে। ওঁরা হাতিগির্জা পাহাড়ের দিক থেকেই আসছিলেন জঙ্গল দেখে-টেখে। যুধিষ্ঠির, ড্রাইভিং সিট থেকে নেমে, ঘুরে গাড়ির পিছন দিকে দুপা সামনে গিয়ে, বাঁদিকে মুখ করে উবু হয়ে হিসে করতে বসল। গ্রামের মানুষেরা শহুরেদের মতো দাঁড়িয়ে হিসি করে না। পুরুষরাও বসেই হিসি করে। এমন সময়ে হঠাৎ যুধিষ্ঠিরের চোখ পড়ল পথের ধুলোর উপরে। বাঘের পায়ের দাগ। একেবারে টাটকা। হিসি করতে করতেই সে চেঁচিয়ে মহান্তিবাবুকে ডেকে বলল, চঞ্চল আসন্তি মহান্তিবাবু, বাঘটা এইঠি অছি।
সে কথা শুনে পট্টনায়েকবাবু গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে ছেলে এবং মহান্তিবাবু দুজনেরই উদ্দেশে হাঁক পেড়ে চললেন, চাল যুধিষ্ঠির! চালন্তু মহান্তিবাবু। চঞ্চল পলাইবি। আউ এঠি রহি হেব্বনি।
যুধিষ্ঠির যখন হিসি করা সেরে বাঁদিক থেকে এসে গাড়ির পিছন ঘুরে গাড়ির ডান দিকের ড্রাইভিং সিটে উঠতে যাবে, ঠিক তখুনি বাঁদিকের জঙ্গল থেকে বাঘ অতর্কিতে এক লাফ দিয়ে যুধিষ্ঠিরের ঘাড়ে পড়ে, তাকে এক ঝটকাতে মাটিতে ফেলে, তার ঘাড় ভেঙে, টুটি কামড়ে ধরে টানতে টানতে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে জঙ্গলের গভীরে চলে গেল পট্টনায়েকবাবু কিছু বোঝার আগেই। বাঘকে দেখে হনুমানেরা হুপ-হুঁপ-হুঁপ করে উঠল। ময়ূর ডেকে উঠল কেঁয়া-পেঁয়া করে। মহান্তিবাবু ধপ করে কিছু একটা মাটিতে পড়ার শব্দ শুনে গড়গড়াটা হাতে নিয়ে উর্ধশ্বাসে দৌড়ে এলেন গাড়ির দিকে। এবং ওই বীভৎস দৃশ্য দেখলেন।
.
ঋজুদা বলল, তিতির তোকে কিন্তু বাংলোতে রেখেই যাব।
কেন?
গোয়েন্দাগিরিতে তুই রুদ্রর চেয়ে অনেক দড়, কিন্তু এইরকম সাংঘাতিক মানুষখেকো বাঘকে পায়ে হেঁটে গিয়ে মারা সত্যিই বড় বিপজ্জনক। ভটকাই এবারে এলে ওকেও নিয়ে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই উঠত না। তা ছাড়া, বন্দুক তো মাত্র দুটো। তাও গুলিগুলোর যা চেহারা দেখলাম, সময়-বিশেষে ফুটলে হয়। অন্য একটা ভাল বন্দুক থাকলেও না হয় কথা ছিল। রাগ করিস না। ভুলও বুঝিস না আমাদের। প্লিজ। তুই বাংলোতে বসে বই পড় বা পাখির ডাক শোন। আজ রাতেই দেখতে পাবি সামনের বিস্তীর্ণ ধানখেতে হাতির পাল নামবে এসে বাঘমুণ্ডা আর হাতিগির্জা পাহাড়ের দিক থেকে। ততক্ষণে, আশাকরি আমরাও অক্ষত অবস্থাতে ফিরে এসে তোর পাশে বসে হাতি দেখব।
কখন ফিরবে তোমরা?
তা কী করে বলব?
টর্চ নিয়ে যাও। আর জলের বোতল।
নিয়েছি। তবে দিনে দিনেই ফিরে আসার চেষ্টা করব। অন্ধকারে মানুষখেকো বাঘের সঙ্গে পায়ে হেঁটে মোকাবিলা করার মতো বাহাদুর আমি নই। জিম করবেট তো সকলে নয়।
বলেই বলল, চললাম রে তিতির।
আমি হাত তুললাম তিতিরের দিকে।
তিতির বলল, গুড লাক। গুড হান্টিং।
পট্টনায়েকবাবু একেবারেই ভেঙে পড়েছেন। তিনি পুরুণাকোটের বড় চায়ের দোকানটার সামনের বেঞ্চিতে আধশোওয়া হয়ে বসেছিলেন আর তার সামনে পুরুণাকোটের অনেকেই দাঁড়িয়ে বসে ছিল। ওঁকে সকলেই চিনত এবং ওদের মধ্যে কেউ কেউ ওঁর কাছে কাজও করেছে বিভিন্ন সময়ে। উনি কেবলই বিলাপ করছিলেন: আমি যুধিষ্ঠিরের মাকে গিয়ে কী বলব! এই পোড়া মুখ দেখাব কি করে। মহান্তিবাবু পাশে বসে তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু সান্ত্বনা কি দেওয়া যায় সদ্য পুত্রহারা বাবাকে? তা ছাড়া যে ছেলের মৃত্যু এমন বীভৎসভাবে হয়েছে, এমন মর্মান্তিকভাবে। বাবারই চোখের সামনে।
পট্টনায়েকবাবুর ড্রাইভারের সঙ্গে স্থানীয় দুজন সাহসী লোক সামনের সিটে বসল। আমি, ঋজুদা আর একনলা গাদা বন্দুকধারী শিকারি, মাঝবয়সি, ফরসা, বেঁটে, যার নাম হট, সেও। ঋজুদা ড্রাইভারকে বলল, তোমরা কেউ গাড়ি থেকে নামবে না।
তাদের কারুরই মুখের ভাব এবং নিঃসাড় অবস্থা দেখে অবশ্য আদৌ মনে হল না যে তারা একজনও গাড়ি থেকে নামবার জন্য ছটফট করছে। বিশেষ করে ড্রাইভার তো নয়ই, গাড়ির পিছনের সিটে বসে যুধিষ্ঠিরের স্বর্গযাত্রা সেও তো চাক্ষুষ করেছিল। যুধিষ্ঠিরের পতনের পর সেই তো গাড়ি চালিয়ে, বিহারে যাকে বলে টিকিয়া উড়ান চালিয়ে রুদ্ধশ্বাসে পুরুণাকোটে এসে পৌঁছেছিল। আধঘণ্টার পথ দশ মিনিটে।
এই ‘টিকিয়া উড়ান’ কথাটা ঋজুদার কাছ থেকেই শেখা। হিন্দি কথা। চালক যখন এত জোরে গাড়ি চালায়, বিশেষ করে জিপ যে, তখন তার টিকিটা মাথার পিছনে হাওয়ার তোড়ে পতাকার মতো খাড়া হয়ে বুনো শুয়োরের লেজের মতো উড়তে থাকে। গাড়ি বা জিপের সেই উদ্দাম গতিকেই বলে ‘টিকিয়া উড়ান।
একটুক্ষণ পরেই ড্রাইভার ক্যাম্পের সামনে আমাদের নামিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল। গাড়িটার সাইলেন্সার পাইপে ফুটো আছে একটা, ফাস্ট রেসিং-এর ফরমূলা কার-এর মতো কান-ফাটানো আওয়াজ করে চলবার সময়ে। গ্রামাঞ্চলে অনেক গাড়ির মালিকের ধারণা আছে, এত টাকা দিয়ে গাড়িই যখন কিনেছি তখন তা নিঃশব্দেই যদি চলল তা হলে জানান দেওয়া যাবে কী করে যে তিনি গাড়ি চড়ছেন! কিন্তু জঙ্গলের কিছু জানোয়ার, বিশেষ করে হাতি এই ভটভট আওয়াজকে এবং মোটর সাইকেলের আওয়াজকেও বিশেষ অপছন্দ করে এবং অনেক সময়ে রে-রে-রে করে তেড়ে আসে, যেমন আসে শহরের পথের কুকুরও। এই ছিদ্রিত শব্দ তাদের irritate করে, চুলকানির মতো।
পথপাশের একটা বড় কালো পাথরে বসে আমরা যার যার বন্দুক এবং গুলি দেখে নিলাম। ব্রিচ ভেঙে বন্দুকটা লোডও করে নিলাম। ঋজুদার শিক্ষা মতো ডান ব্যারেলে এল জি এবং বাঁ ব্যারেলে বুলেট পুরি শটগানে যদি বন্দুকের ব্যারেলে ‘ডাবল চোক’ থাকে। এই বন্দুক বেলজিয়ান। ১২ বোরের আর ঋজুদারটা অঙ্গুলের ঠিকাদার বিমলবাবুর। ইংলিশ টলি বন্দুক। বন্দুকটার চেহারা ছবি ভাল। যত্নে রাখেন মনে হয়। আমার বন্দুকটার দু ব্যারেলেই ময়লা আছে। শেষবার গুলি ছুঁড়ে আর পরিষ্কার করা হয়নি। ভাল শিকারি ও যত্নবান মানুষে নিজের নিজের বন্দুককে নিজের বউ-এর চেয়েও আদরে রাখেন। এই বন্দুকের মালিক বন্দুকেরই যদি এত অযত্ন করেন তবে বউ-এর কী অযত্নই না করেন! ভেবে শিহরিত হলাম, নিজের বউ না-থাকা সত্ত্বেও।
বুলেট বলতে আমার স্টক-এ একটামাত্র লেথাল বল। ইন্ডিয়ান অর্ডন্যান্স কোম্পানির। আমাদের দেশে বন্দুক ভালই তিৈর হয়, কিন্তু গুলি, বিশেষ করে ছররা গুলির এমনই জারিজুরি যে বুনো হাঁস পর্যন্ত গায়ে লাগলে ডানা ঝেড়ে অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে ঝুরঝুর করে ফেলে দেয়। এক দানা ছররাও ডানা ভেদ করে শরীরে প্রবেশ করে না। জানি না, এখন হয়তো ইন্ডিয়ান অর্ডন্যান্সের গুলির মান উন্নত হয়েছে। গুলিগুলোতে শ্যাওলা জমে গেছে, ফাঙ্গাস। কে জানে, কত বসন্ত এবং বর্ষার সাক্ষী এরা! পিতলের ঝকঝকে ক্যাপ নীল হয়ে গেছে দীর্ঘদিনের অবহেলায়।
আমি মাঝেমধ্যে দায়ে পড়লে মিথ্যা কথা বলি না এমন নয়। তাই এই–ফোঁটা গুলির বন্দুক হাতে করে হতভাগা বাঘের ভোগে লেগে আমারও সত্যবাদী যুধিষ্ঠির হবার কোনও বাসনা আদৌ ছিল না। কিন্তু কী করা যাবে। এই হাতিয়ার হাতেই যথাসাধ্য করতে হবে। একটা মানুষকে শব বানিয়ে সেই রাক্ষস এখন তাকে খাচ্ছে।
ঋজুদার মুখ দেখে মনে হল সেও এমনই ভাবছিল গুলি লোড করতে করতে। কিন্তু কী আর করা যাবে! নিজেদের হাতের বন্দুক রাইফেল ছাড়া মানুষখেকো বাঘের মোকাবিলা করা সত্যিই বড় অস্বস্তিকর।
আমাদের সঙ্গী মিস্টার হট অথবা হটবাবুর পরনে একটা গেরুয়া খেটো ধুতি। গায়ে একটা ঘোর লাল রঙের গেঞ্জি। তার উপরে ঘোরতর বেগুনে রঙের বিনুনি করা র্যাপার। ঋজুদার নিম্নাঙ্গে হালকা ছাইরঙা ফ্লানেলের ট্রাউজার এবং উপরে বিস্কিট রঙের জমির উপরে অতি হালকা সবুজ স্ট্রাইপের ব্লেজার। আমি পরেছি একটা ফিকে নীল জিনস তার উপরে বড় মামিমার বুনে দেওয়া লেমন ইয়ালো রঙা ফুলহাতা পোলো-নেক সোয়েটার, টেনিস খেলার সাদা ফ্রেড-পেরি গেঞ্জির উপরে। শিকারিদের সাজ-পোশাক দেখলে বাঘ এমনিতেই ভিরমি খাবে। গুলি আর করতে হবে না। তা কী আর করা যাবে। এখানে এসে যে মানুষখেকো বাঘের মোকাবিলা করতে হবে তা কে জানত আগে।
হটবাবু লোকটার ভয়ডর একটু কমই আছে। বটুয়া থেকে বের করে সেজে দুটো অখয়েরি গুণ্ডি মোহিনী পান মুখে দিয়ে অনেকখানি গুণ্ডি ফেলে বলল, চলন্তু, জীবা।
অকুস্থলে পৌঁছে হটবাবু পাথরে বসে মনোযাগ সহকারে তার গাদা বন্দুক গাদছিল। তিন আঙুল মতো বারুদ গেদে তারপর সামনে সিসের একটা রেকটাঙ্গুলার তাল (আদৌ গোল নয়) গেদে দিয়ে সে বাঘের বাপের নাম খগেন’ করবে বলে দৃঢ়প্রত্যয় হয়ে রওয়ানা হবে বলে তৈরি যখন হচ্ছে তখন ঋজুদা তার টগবগে উত্তেজনাতে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়ে বলল, হটবাবু, আপনি এখানেই থাকুন। এই বড় আমগাছটার উপরের ডালে চড়ে দেখুনতো কিছু দেখতে পাচ্ছেন কি না! আপনি এখানে উচ্চাসনে বসে আমাদের বলতে পারবেন কিছু দেখতে পাচ্ছেন কি না এবং যা দেখতে পাচ্ছেন তা কোথায়?
হটবাবু হতাশ গলাতে বললেন, আমি সঙ্গে যাব না?
ঋজুদা মাথা নেড়ে বলল, না। আপনি এখান থেকে আমাদের ডিরেকশন দিলে ভারী সুবিধা হবে। আপনিই তো হলেন গিয়ে আমাদের ডিরেক্টর। যেমন ডিরেকশন আপনি দেবেন আমরা তেমন তেমন কাজ করব।
আবারও বুঝলাম, মানুষটা সাহসী। বাঘটার টাটকা ক্রিয়াকাণ্ড সম্বন্ধে সব জেনেও আমাদের সঙ্গে যাবার জন্য উন্মুখ।
এই ডিরেক্টর শব্দটা হটবাবুর খুব মনে ধরল।
তিনি বললেন, ঠিক আছে। আপনি যেমন বলবেন, তেমনই হবে। বলেই, তিনি বড় আমগাছটাতে ওঠার তোড়জোড় শুরু করলেন। ঋজুদা বলল, আপনি উঠে গেলে তবেই আমরা এগোব।
আচ্ছা। উনি বললেন।
ঋজুদা বলল, আমরা এই গাছের নীচে এসে আপনাকে আওয়াজ দিলে তখনই তাড়াতাড়ি নেমে আসবেন। আর আমরা না-আসা পর্যন্ত এই গাছ থেকে একেবারেই নামবেন না। বুঝেছেন? একেবারেই নয়। এই বাঘটা কিন্তু মহাধূর্ত।
আইজ্ঞাঁ।
মনমরা হয়ে বললেন, হটবাবু।
আমরা দুজনে আগে পরে সিংগল ফরমেশানে এগিয়ে যেতে যেতে যেখানে বাঘটা যুধিষ্ঠিরের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে তার টুটি কামড়ে তাকে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে গেছে সেখানে মনোযোগ দিয়ে পথের লাল ধুলোর উপরে বাঘের থাবার দাগ ভাল করে লক্ষ করলাম।
আমি বললাম, ঋজুদা, এ তো বাঘিনী!
হু। তাতে কী হয়েছে! বাঘ হলেও মানুষখেকো, বাঘিনী হলেও তাই।
ঋজুদা পাইপটার ছাই ঝেড়ে বুক পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল।
তারপরে নিচু গলায় বলল, আরও একটু গিয়ে আমরা ব্রাঞ্চ-আউট করে যাব। বুঝেছিস। তুই যদি আগে দেখতে পাস তা হলে আমার জন্য এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করবি। আমি যদি কাছাকাছি থাকি তবে হাতের ইশারাতে বলবি বাঘ কোনদিকে গেল, মানে, যদি এক গুলিতে না পড়ে। তবে একদমই হড়বড় করবি না। বড় বাঘিনী, তার উপর ধূর্ত মানুষখেকো। ভাইটাল জায়গাতে গুলি করবি। রেঞ্জ-এর বাইরে গুলি মোটেই করবি না। যত কাছ থেকে করতে পারিস ততই ভাল। বন্দুক ও গুলি কোনওটার উপরেই তো ভরসা নেই। দুই-ই তো পরস্মৈপদী। আমি যদি আগে দেখতে পাই তো আমিও গুলি করব। এই সুযোগ নষ্ট হলে সাত দিনের মধ্যে আর হয়তো সুযোগ পাওয়াই যাবে না। বুঝেছিস। তোদের তো ঘুরিয়ে সব জায়গা দেখাতেও হবে, যেজন্য এবারে আসা!
হুঁ। আমি বললাম।
তারপর যতদূর ড্র্যাগ-মার্ক আছে, রক্তের দাগ আছে ততদূর আমরা আগে-পিছে করে এগোতে থাকলাম। ড্র্যাগ-মার্ক দেখে বোঝা গেল যে, বাঘটা যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে পথের ডানদিক থেকে পথ পেরিয়ে বাঁদিকের জঙ্গলে গেছে। প্রায় সমকোণে। তার মানে নন্দিনী নালার দিকেই নিয়ে গেছে লাশ। সেই পথে খাওয়া সেরে, জল খেয়ে বনের গভীরে কোথাও রোদের মধ্যে আরামে ঘুমোবে।
এখন নালার এপাশেই আছে না, নালা পেরিয়ে ওপাশে গেছে, তা দেখতে। হবে। যা শীত! দশটা বাজে কিন্তু এখনও জমির উপরের শিশির-ভেজা ঘাস ও ঝোপঝাড়ের পাতা পুরোপুরি শুকোয়নি। বড় গাছের পাতাগুলো অনেক বেশি রোদ পায়। তারা প্রায় শুকিয়ে এসেছে। একটা মস্ত কুচিলা গাছে বসে অনেকগুলো বড়কি ধনেশ হ্যাঁক-হ্যাঁক, হক্ক-হক্ক করছে। ভারী কর্কশ ডাক এই পাখিগুলোর।
পথের লাল ধুলোতে লাশ হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগ এবং রক্ত পড়েছিল। তখনও রক্ত শুকোয়নি। তখনও দুজনে এক সঙ্গেই এবং কাছাকাছিও ছিলাম। যখন বাঘের বা লাশের চিহ্ন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না তখনই আমরা আলাদা হয়ে যাব দুদিকে। এমনই ঠিক ছিল।
বনের গভীর থেকে ময়ূর ডাকছে। দুটো কুম্ভাটুয়া পাখি, ইংরেজিতে যাদের নাম Crow Pheasant, বাদামি আর কালো, বড় লেজ-এর গুব-গুব-গুব-গুব করে ডেকে বনের আনোছায়ার রহস্যময়তা আরও যেন বাড়িয়ে দিচ্ছে। রাতের বেলা। এদের ডাক শুনলে বুক দুরদুর করে। কেন কে জানে! কপারস্মিথ পাখি ডাকছে। টাকু-টাকু-টাকু-টাকু করে। আর তার দোসর সাড়া দিচ্ছে নন্দিনী নালার ওপার থেকে। শীতের সকালের মন্থর হাওয়াতে বাঁশবনে নিচুগ্রামে স্বগতোক্তির মতো কটকটি আওয়াজ উঠছে। বাঁশের গায়ের হলুদ আর পেঁয়াজখসি রঙের হালকা, মসৃণ ফিনফিনে খোলস উড়ছে ঝিরিঝিরি করে বয়ে-যাওয়া ঠাণ্ডা হাওয়ায়। চারিদিকে সবুজের সে কী সমারোহ! সবুজ যে কত রকমের হতে পারে তা জানতে হলে আমাদের দেশে নয়তো পশ্চিম আফ্রিকাতে যেতে হয়। পরতের পর পরত, গাঢ় থেকে ফিকে, ফিকে থেকে গাঢ়, কত বিভিন্ন ছায়ার সবুজ যে আছে। এখানে।
আমরা নালার পারে এসে দাঁড়ালাম। বাঘিনী লাশটাকে নিয়ে প্রস্তরময় এবং বালুময় নন্দিনী নালা পেরিয়ে ওপারে চলে গেছে। নানা পাথরের উপরে এবং বালিতে রক্তের দাগের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরকে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগ আর বাঘিনীর থাবার দাগ। বালির উপরে যুধিষ্ঠিরের রক্তমাখা ধুতি, পাঞ্জাবি, আন্ডারওয়্যার এবং আলোয়ান বিভিন্ন জায়গাতে, আগে-পরে ফালাফালা হয়ে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। চটি-জোড়া অবশ্য যেখানে বাঘ তার ঘাড়ে পড়েছিল সেখানেই উল্টে পড়েছিল। নদীর ওপারের কোনও নিভৃত জায়গাতে নিয়ে গিয়ে সে খাচ্ছে যুধিষ্ঠিরকে অথবা খেয়েছে অথবা ফেলে চলে গেছে জঙ্গলের গভীরে কোথাও গাছ-গাছালির চন্দ্রাতপের নীচে লাশটাকে, শকুনের চোখের থেকে আড়াল করে, পরে এসে খাবে বলে।
এমন সময়ে, হঠাৎ ঋজুদা একটা শিস দিল। বুলবুলির শিস-এর মতো।
ঋজুদার চোখকে অনুসরণ করে দেখলাম যে বাঘিনীর থাবার দাগ। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে কিছুটা বাঁদিকেই নদীর বালির উপরে।
বাঘিনী কি নদী পেরিয়ে বাঁদিক দিয়ে উঠে এপারে এসেছে লাশ ফেলে রেখে? বালির উপরে দাগগুলো ধেবড়ে রয়েছে। তার মানে, খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে এসেছে সে।
কতক্ষণ আগে নদীটা পেরিয়ে এদিকে এসেছে তা কে জানে। আমাদের গাড়ির শব্দ শুনে বা আমাদের কথাবার্তা শুনেই কি সে কী ব্যাপার’ তা দেখতে এসেছে? নাকি, তাকে আমরা অনুসরণ করে এখানে এসে পৌঁছবার একটু আগেই নদী পেরিয়ে এদিকে এসেছে। গাড়ির আওয়াজ এবং আমাদের এখানে আসার শব্দ পেয়ে অন্য বাঘ হলে তার বনের আরও গভীরের নিরাপত্তাতে চলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল লাশ নিয়ে অথবা না-নিয়েই, কিন্তু সে না পালিয়ে, আবারও এপারেই এসেছে। আমাদের বেয়াদবির উচিত শিক্ষা দেবার জন্যেই কি? না, নিছক ঔৎসুক্যরই কারণে?
সুন্দরবনের মানুষখেকোরাও নাকি এরকম। মানুষের ভয় তাদের চলে গেছে। পারে নৌকো ভিড়লে, এমনকী বনবিভাগের দেওয়া আছাড়ি পটকার শব্দ শুনলেও, তারা পালিয়ে না গিয়ে, সেই শব্দর কাছে আসে, সুযোগ খোঁজে, মানুষ ধরার। বাঘের মতো তীব্র ঔৎসুক্য খুব কম প্রাণীরই আছে। ঋজুদা বলে ‘inquis itivness’-ই হচ্ছে শিক্ষিত মানুষের লক্ষণ। এই জন্যই বাঘকে ঋজুদা খুবই জ্ঞানী বিবেচনা করে। পৃথিবীর সব চাইতে সাহসী প্রাণী হিসাবে তো করেই।
খবরের কাগজের ভাষায় যাকে বলে কিংকর্তব্যবিমূঢ়, তাই হয়ে আমরা দুজনে যখন সিচুয়েশনটা সাইজ-আপ করছি ঠিক সেই সময়েই পট্টনায়েকবাবুর পুরনো ক্যাম্পের দিক থেকে গদ্দাম করে একটা গুলির আওয়াজ হল। বন্দুকের গুলি তো ফুটল না, যেন গাঁঠিয়া ফুটল। সে আওয়াজে মেদিনী কম্পমান হল। এবং সঙ্গে সঙ্গে হটবাবুর গলা ফাটানো চিৎকার শোনা গেল, স্যর। স্যর। সে বাঘ সে পাখের গন্ধা। সাবধান! সাবধান!
গুলির আওয়াজ এবং হটবাবুর চিৎকার শুনে আমরা দুজনে দুপাশে সরে গিয়ে পজিশন নিলাম বসে পড়ে। ঋজুদা আমাদের পিছনের রাস্তা এবং পাশের জঙ্গলে চোখ রাখল আর আমি নদীর দিকে।
পট্টনায়েকবাবুর পুরনো ক্যাম্পটা থেকে আমরা বড়জোর পাঁচশো গজ এসেছি। হটবাবুর গুলি খেয়ে অথবা না-খেয়ে বাঘের আমাদের কাছে পৌঁছতে অতি সামান্য সময়ই লাগার কথা। অথচ বনে অথবা নদীতে কোনওই শব্দ নেই।
গুলির শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দূর থেকে অগণ্য হনুমান হুপ-হুঁপ-হুঁপ করে উঠেছিল। অসংখ্য অদৃশ্য পাখি উত্তেজিত হয়ে ডালে ডালে নাচানাচি করতে করতে ডাকছিল। কিন্তু তাদের কলরবও এখন থেমে গেছে পুরোপুরি। এখন মৃত্যুর নৈঃশব্দ্য চারদিকে। নন্দিনী নালার জলের চলার শব্দই শুধুই ছিদ্রিত করছে দিনমানের সেই ভৌতিক গা-ছমছম নিস্তব্ধতাকে।
এমন সময়ে হঠাৎই জলে একটা ছপছপ শব্দ শুনতে পেলাম। শব্দটা এল ঋজুদা যেদিকে ছিল, সেই বাঁদিক থেকেই। নন্দিনী নালা সেখানে একটা ঠিক পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি বাঁক নিয়েছিল।
আমি যেখানে ছিলাম সেখান থেকে নদীর ওপাশটা দেখতে পাচ্ছিলাম না। ছপছপ শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই ঋজুদা দ্রুত নদীর দিকে এগিয়ে গিয়ে Prone Position-এ আগাছা-টাগাছার উপরেই শুয়ে পড়ল। তাতে যে শব্দ হল তা নিশ্চয়ই বাঘের অতি-সজাগ কান এড়াল না। তারপর…।
বন্দুকটাকে সোজা করে ঋজুদা চকিতে নিশানা নিয়ে গুলি করল।
কী হল বোঝা গেল না। ততক্ষণে আমিও ঋজুদার দিকে দৌড়ে গেছি। কিন্তু ঋজুদা, আমি পৌঁছবার আগেই স্লিপ খাবার মতো করে নদীর বুকে নেমে পড়েছে। তাকিয়ে দেখি, বাঘিনী, দুটো পাথরের মাঝে নদীর জলে পড়ে রয়েছে এবং তার শরীরের রক্ত নদীর বহমান জলকে ধীরে ধীরে গোলাপি করে দিয়ে বইছে।
ভাবলাম, তাহলে হটবাবুর কামানের গুলি কি ফসকে গেল? ঋজুদার গুলিই লাগল এখন? ঋজুদা, জল, বালি ও পাথর এক এক লাফে টপকে-টপকে বাঘিনীর দিকে এগোচ্ছিল। উদ্দেশ্য, বাঘের খুব কাছে গিয়ে তাকে আবার গুলি করা। আমিও ঋজুদার পিছন পিছন ছুট লাগালাম। বাঘিনী থেকে যখন হাত কুড়ি দূরে তখন ঋজুদা দাঁড়িয়ে পড়ে বাঁদিকের ব্যারেল ফায়ার করল। কিন্তু গুলি ফুটল না। যে বাঘিনী মরে গিয়েছিল ভেবেছিলাম, সে-ই মুহূর্তের মধ্যে ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মতো ছিটকে উঠে, উড়ে এল ঋজুদার উপরে। আমি ঋজুদার হাত দুয়েক ডানদিকে ছিলাম এবং হাত পাঁচেক পিছনে। বন্দুক তুলে বাঘিনীর লাফানোর সঙ্গে সঙ্গে আমি ডানদিকের ব্যারেল ফায়ার করলাম উড়ন্ত বাঘের গলা লক্ষ্য করে। ডানদিকের ব্যারেলে ভাগ্যিস এল জি. পুরেছিলাম। এল জি-র বড় বড় দানাগুলো তার গলাতে ও ঘাড়ে প্রচণ্ড ধাক্কা দিল।
শর্ট-রেঞ্জে শটগানের মতো কার্যকরী আর কিছুই নয়। হাই-ভেলোসিটি রাইফেলের গুলি বাঘের শরীর এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়ে চলে যায় বটে, কিন্তু তার আগে বাঘও সহজে মেরে দিয়ে যেতে পারে শিকারিকে। শর্ট-ডিসট্যান্সে, রাইফেলের গুলি কিন্তু ধাক্কা দিয়ে আহত বিপজ্জনক জানোয়ারকে উলটে ফেলে দিতে পারে না। বন্দুকের গুলি পারে।
এত করেও ঋজুদাকে বাঘিনীর হাত থেকে বাঁচাতে পারলাম না। দু’হাত আর দু’পা প্রসারিত করে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নখ ছড়িয়ে বাঘিনীটা ঋজুদার উপরে এসে পড়ল। বন্দুকের গুলির স্টপিং-পাওয়ার short-range-এ সত্যিই মারাত্মক। তাই বাঘিনী তার শরীরের কয়েকমণ ওজন নিয়ে ঋজুদার বুকে পড়ে তাকে আহত করল বটে কিন্তু তার দম ফুরিয়ে এসেছিল তখন। শুধু গতিজাড্যতেই তার শরীরটা এসে পড়েছিল ঋজুদার উপরে, তার আক্রমণে জোর ছিল না একটুও। বাঘিনী, ঋজুদাকে বালি আর জলের মধ্যে ধাক্কা দিয়ে ফেলে নিজেও বালির মধ্যেই পড়ে গেল। ঋজুদার গা ঘেঁষে।
আমি কোনও ঝুঁকি না নিয়ে দৌড়ে গিয়ে তার বাঁ কানের ফুটোর কাছে ব্যারেল ঠেকিয়ে বাঁদিকের ব্যারেল ফায়ার করলাম। খট করে একটা শব্দ হল। কিন্তু গুলি ফুটল না।
কিন্তু বাঘিনী তখন স্বর্গলাভের জন্য ব্যাকুল। কানের কাছে সেই খট শব্দেই সে চোখ দুটো বন্ধ করে মাথাটা এলিয়ে দিল। এমনই ভাবে এলাল। যেন ঋজুদাকে কোল বালিশ করেই শুতে চায়।
ইতিমধ্যে ক্যাম্পের দিক থেকে গদ্দাম করে আরেকটা আওয়াজ হল হটবাবুর গাদা বন্দুকের। সে আওয়াজ পুরুণাকোট অবধি পৌঁছবার দরকার ছিল না। তার আগেই আগেপিছে পরপর তিনটা গুলির আওয়াজে পট্টনায়েকবাবু এবং মহান্তিবাবু নিজেরাই গাড়িতে বসে ড্রাইভারকে এবং অন্য একজনকে নিয়ে জোরে গাড়ি চালিয়ে ক্যাম্পের কাছে এসে পৌঁছেছিলেন। পৌঁছেই হটবাবুর কাছে ফাস্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট নিয়ে গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন পুরুণাকোট থেকে সকলকে আসার জন্য খবর দিতে।
ঋজুদার সমস্ত শরীর রক্তে ভিজে যাচ্ছিল। তবু উঠে বসে ডান হাত দিয়ে ডান কানে হাত দিয়ে বলল, এই কান ধরলাম, আর কোনওদিন অচেনা বন্দুক আর অচেনা গুলিতে এ জীবনে শিকার করব না। ভাগ্যিস তোর গুলিটা ফুটেছিল নইলে আমাকে বাঘিনী ছিঁড়ে খুঁড়ে দিত।
তোমার কিন্তু আসলে হয়নি কিছুই। নখও তেমন ঢোকেনি ভিতরে। তোমার মোটা টুইডের কোটটা খুব কাজে দিয়েছে।
তা ঠিক। আঘাত গুরুতর নয় অবশ্যই। কিন্তু তবু কথায় বলে, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা।
তুমি নিজে হেঁটে যেতে পারবে?
আমি ঋজুদাকে জিজ্ঞেস করলাম।
তারপর স্বগতোক্তি করলাম, রক্ত যাতে বন্ধ হয় তার জন্য কিছু করতে হবে।
মনে হয় তো পারব। তবে একটা shock তো হয়েছেই। দাঁড়া। পাথরে হেলান দিয়ে বসে পাইপটা ধরাই।
ইতিমধ্যে হটবাবুর সঙ্গে পট্টনায়েকবাবু, মহান্তিবাবু আর পট্টনায়েক বাবুর ড্রাইভার লাফাতে লাফাতে নদীর মধ্যে নেমে এলেন।
পট্টনায়েকবাবু বললেন, আমার ছেলের খুনের বদলা নিতে গিয়ে আপনি নিজের প্রাণটাই দিয়ে বসেছিলেন ঋজুবাবু। কী করে যে কৃতজ্ঞতা জানাব। বলেই কেঁদে ফেললেন ঝরঝর করে।
মহান্তিবাবু নদীর পারে ফোঁটা জংলি গ্যাঁদার পাতা কোঁচড় ভরে ছিঁড়ে এনে দুহাতে কচলে কচলে তার রস নিংড়ে ফেলতে লাগলেন ঋজুদার ক্ষতগুলির উপরে।
ঋজুদা রাগের গলাতে পট্টনায়েকবাবুকে বললেন, এই গুলিগুলো কার কাছ থেকে এনে দিয়েছিলেন। তাকে আমি গুলি করে মারব। খুনের দায় বাঘিনীর নয়, সেই দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকেরই।
আমি হটবাবুকে বললাম, কোথায় গুলি করেছিলেন আপনি বাঘের শরীরের? বাঘটা এল কোন দিক থেকে?
তা কী আমি জানি! আপনারা চলে যেতেই দেখি বাঘটা ক্যাম্পে মহান্তিবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে পথে পড়ে আপনাদের দিকে গুঁড়ি মেরে এগোচ্ছে। গাছের ওপরে যে তার যম বসে আছে তা তো সে দেখেনি।
হটবাবু তারপরে বললেন, তার মানে, আমরা যখন এখানে কথাবার্তা বলছিলাম বাঘ তখনি নদী পেরিয়ে এসে মহান্তিবাবুর ঘরে চোখের আড়ালে ঢুকে পড়েছিল। কে জানে! হয়তো মহান্তিবাবুর গড়গড়া টানতে এসেছিল।
আমি বললাম, বাঘ নয়, বাঘিনী।
উনি বললেন, ওই হল। ডোরাকাটা তো!
তারপর?
তারপর কী? আমি দেখলাম হারামজাদি তো এবারে আপনাদের একজনকে ধরবার তালে আছে। তাই আর কালবিলম্ব না করে দেগে দিলাম আমার একনলি গাদা বন্দুক তার শিরদাঁড়া লক্ষ করে।
গুলিটা সম্ভবত শিরদাঁড়াতে না লেগে পাশে লেগেছিল।
শিরদাঁড়াতে লাগলে ওইখানেই চিৎপটাং হত। দেখো, একশো গ্রামেরও বেশি সিসে দিয়ে তালের বড়ার সাইজের বল বানিয়ে ছিলাম। আমার বন্দুকের নল সেই প্রায় চারকোনা বল-এর বলে ফেটে যায়নি এই বাঁচোয়া। কিন্তু বাঘিনী বিলক্ষণ বুঝেছে হটকুমার দাস-এর মার কী জিনিস। তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী কেউ কখনও আমার সামনে এ জীবনে আসবে না। মাটিতে বসে পড়েছিল গুলি খেয়েই। তারপর হাঁচোড়-পাঁচোড় করে কোনওক্রমে উঠেই নদী বলে ভোঁ দৌড়। দোনলা বন্দুক আমার কাছে থাকলে পথেই ওকে থাকতে হত।
দোনলা বন্দুক থাকলে কী হত? গুলিই তো ফোটে না! তা ছাড়া এতই যদি আপনার আত্মবিশ্বাস তো এতদিনে বাঘিনীকে মারলেন না কেন?ন’নটা, ন’টা কেন যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে দশজন মানুষ খেল!
হটবাবু কথা ঘুরিয়ে বলেন, ওই বটকেষ্ট দাস অমনই। মহা কেপ্পন। তা ছাড়া ও তো মারে চুরি করে হরিণ কুটরাই। বাঘের সামনে গেছে কখনও? ধুতি হলুদ হয়ে যাবে না!
তারপর বললেন, আমি এমনি চিতা বা বড় বাঘও মেরেছি কিন্তু এই মানুষখেকোর হরকৎ দেখে আমার রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। আপনারা এসে বল দিলেন। তাই বল পেয়ে বন্দুকে বল দেগে সঙ্গে এলাম। একা আমার সাহসে কুলোত না। আমিও ফাইটার কিন্তু আমার একজন ক্যাপটেন লাগে। ক্যাপটেন ছাড়া আমি অচল।
একটু পরে পট্টনায়েকবাবুর গাড়ির পিছনে পিছনে জিপ চালিয়ে তিতিরও এসে গেল।
ঋজুদা তিতিরকে দেখে উঠতে গিয়েই পড়ে গেল। কে জানে! কী ধরনের আঘাত হয়েছে। হার্ট কী লাংস-এ বাঘিনীর নখ ঢুকে গেল না তো? বাঁ কাঁধ আর বাহুর সংযোগস্থলে বেশ ভালই জখম হয়েছে বোঝা গেল। বাঁ হাত তুলতে বা নাড়াতে পারছিল না।
মহান্তিবাবুর নেতৃত্বে একদল নদী পেরিয়ে গেল যুধিষ্ঠিরের লাশের যা অবশিষ্ট আছে, তা খুঁজে আনতে। আরেক দল বাঘকে বয়ে নিয়ে যাবার জন্য কাঠ কেটে দোলার মতো বানাতে লাগল বুনো লতা বেঁধে বেঁধে। আর অন্য একদল তাড়াতাড়ি একটা বাঁশের চালি বানাল। যেমন চালিতে করে মৃত মানুষকে ইলেকট্রিক চুল্লিতে ঢোকানো হয়। সেই চালিতে করে ঋজুদাকে জিপ অবধি বয়ে নিয়ে যাবে তারা। মানুষটা তো আর রোগা পটকা নয়। আমাদের ঋজুদাও তো বাঘই।
বাঁশের চালিটা দেখে আমার মন খারাপ হয়ে গেল। তিতির আমার চোখের দিকে তাকাল। আমি ওর চোখের দিকে।
তিতির এসে ঋজুদাকে ধরল, আমি অন্য দিকে। তিতির তার লালরঙা সিল্কের স্কার্ফটা, যেটা ও মাথায় বেঁধে বসে থাকে জিপে যাওয়া-আসার সময়ে এবং যার উপরে হলুদ আর লাল ফুল ফুল প্রিন্টের কাপড়ের টুপিটা পরে উড়ন্ত চুলকে বশ করার জন্য, সেটা ঋজুদার বাঁ কাঁধে জড়িয়ে দিল। রক্তের লাল আর স্কার্ফের লাল মিশে গেল।
হঠাৎ ঋজুদা থরথর করে কাঁপতে শুরু করল। বলল, শীত করছে কেন রে আমার?
আমার ভীষণই ভয় করতে লাগল।
ঋজুদাকে তুলে নদী ধরে ওরা ক্যাম্প বরাবর চলতে লাগল যাতে পথে উঠতে সুবিধা হয়। ক্যাম্পের কাছে ঘাট মতো করা ছিল। যত কাবাড়ি চান করত, খাবার জল রান্নার জল সব নিত তো ওই ঘাট দিয়ে নেমে নদী থেকেই।
এমন সময়ে পট্টনায়েকবাবু দৌড়ে চলে গেলেন তাঁর গাড়ির দিকে। ঋজুদাকে আমরা সকলে মিলে ক্যাম্পের সামনের ফাঁকা জায়গাতে যখন উঠিয়ে আনলাম তখন পট্টনায়েকবাবু একটা বোতল নিয়ে দৌড়ে এলেন। দেখলাম গায়ে লেখা আছে Doctor’s Brandy। ঋজুদার ক্ষতস্থানগুলোতে একটু একটু করে ঢেলে দিলেন পট্টনায়েকবাবু। তারপর বোতলটা ঋজুদার হাতে দিয়ে বললেন, ওষুধ। একটু একটু করে খান ঋজুবাবু।
তারপরই হটবাবু অবিশ্বাস্য কাজ করলেন। হাঁক পাড়লেন, হাড়িবন্ধু। হাড়িবন্ধু কুয়ারে গন্ধে?
হাঁ আইজ্ঞাঁ। বলেই এক বিকটদর্শন সাড়ে ছ’ফিট লম্বা দৈত্যপ্রমাণ মানুষ–তার নাক নেই, যেখানে নাক থাকার কথা সেখানে বিরাট দুটি ফুটো–এসে দাঁড়াল। বুঝলাম, ভালুকে তার নাক খুবলে নিয়েছে। নীচের ঠোঁটেরও কিছুটা। হটবাবু আমাদের সকলকে সরে যেতে বললেন দূরে, তারপর হাড়িবন্ধুকে বললেন, ভালো করি কি বাবুকি সব্ব ক্ষতেরে মুত্বি পকা।
আমরা সরে যেতেই হতভম্ব ঋজুদাকে আরও হতভম্ব করে সেই বিশালাকৃতি হাড়িবন্ধু তার বিশালাকৃতি প্রত্যঙ্গটি বের করে লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে ঋজুদার সর্বাঙ্গে হিসি করতে লাগল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। যেন বাগানে জল দিচ্ছে। তিতির দূরে গিয়ে অন্যদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল।
.
আমরা যখন ঋজুদাকে জিপের পিছনের সিটে শুইয়ে নিয়ে পুরুণাকোটের বাংলোতে এলাম তখন বাংলোর সামনেটা লোকে লোকারণ্য। খুশির জোয়ার বইছে চারদিকে। এতদিন বাঘিনী বাঘঘমুণ্ডার জঙ্গলে যারা কাঠ কাটতে যেত এবং হাতিগির্জা পাহাড়ের দিকে যেত, তাদেরই ধরেছিল। এই প্রথম পুরুণাকোটের এত কাছে নন্দিনী নালার পাশে পট্টনায়েকবাবুর ক্যাম্পের সামনে থেকে দিনমানে এবং মোটর গাড়ির একেবারে পাশ থেকে অন্য মানুষদের সামনেই যুধিষ্ঠিরকে নেওয়াতে পুরুণাকোটে আতঙ্কের ছায়া নেমে এসেছিল। রাতের বেলা তো অলিখিত কার্টু ছিলই, ইদানীং দিনের বেলাতেও মানুষজন বাড়ির বাইরে যেতে সাহস করত না আর। তাই বাঘিনীর মৃত্যুর সংবাদে স্বাভাবিকভাবে আনন্দের জোয়ার বয়ে গিয়েছিল। ৪৫৪
টিকরপাড়া থেকে কটকগামী বাস থামিয়ে মানুষে করতপটা গ্রামে এই সুসংবাদটি দিতে অনুরোধ করল ড্রাইভার আর কনডাক্টরকে। করতপটা’ শব্দটির মানে হচ্ছে করাত দিয়ে চেরা। করাতি বা কাবাড়িদের গ্রাম বলেই গ্রামের নাম করতপটা। লবঙ্গী যাবার পথ ছাড়িয়ে আরও কিছুদূর পরে একটা ছোট নদীর পারে সেই গ্রাম। পথটা নদীর উপর দিয়েই গেছে।
ঋজুদার একটা আচ্ছন্ন ভাব এসেছে। সেটা মোটেই ভাল নয়। পুরুণাকোট বাজারের মধ্যেই অঙ্গুল ও কটক যাবার পথের বাঁদিকে একটা ছোট হাসপাতাল আছে রাজ্য সরকারের। সেখানে ভালুকে নাক কান ছিঁড়ে নেওয়া, সাপের কামড় খাওয়া এবং বাঘ বা চিতার আক্রমণে আহত বা নিহত হওয়া, হাতির লাথি খেয়ে পিলে ফাটা মাথা থ্যাঁৎলানো অথবা বাইসনের বা গাউরের শিঙের গুঁতোতে বিপজ্জনকভাবে আহত মানুষদের প্রায়ই চিকিৎসার জন্য অথবা ডেথ সার্টিফিকেটের জন্য আনা হয়। কখনও বা যাদের নেহাতই মন্দভাগ্য সেইসব মানুষের লাশ চটে-মোড়া অবস্থাতে মাছি ভন ভন করতে করতে গোরুর গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হয় অঙ্গুল বা কটকে। ঈশ্বরের ভরসায় ক্রন্দনাকুল আত্মীয়স্বজনেরা সেই দুর্গন্ধ ফুলে-ঢোল লাশ নিয়ে হা-পিত্যেশ করে বসে থাকে কখন লাশকাটা ঘরের ডাক্তারবাবু আর ডোমেদের দয়া হবে শবব্যবচ্ছেদ করে, যে ঘোরতর মৃত, তাকেই দিন কয় পরে মৃত বলে ঘোষণা করে, একটা সার্টিফিকেট দেবার।
পৃথিবীর খুব কম দেশেই সম্ভবত আমাদের দেশের মতো সাধারণ, সংযোগহীন, গরিব মানুষ মরে গেলেও তার নিস্তার নেই। কী লাশকাটা ঘরে, কী শ্মশানে, ডোমদের এবং অন্যান্যদের হৃদয়বিদারক অত্যাচার চোখে দেখা যায় না।
পুরুণাকোটের হাসপাতালে বেনজিন ডেটল এবং কিছু পেইনকিলার ট্যাবলেট এবং টেডভ্যাক ইনজেকশন ছাড়া ঋজুদার আর কোনও চিকিৎসাই হল না। আমি আর তিতির ঠিক করলাম যে, অঙ্গুলে গিয়ে, অঙ্গুল তো কটকের পথেই পড়বে, বিমলবাবুকে সঙ্গে নিয়ে আমরা সোজা ভুবনেশ্বরে চলে যাব। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়ে সন্ধের প্লেন ধরে, যে-প্লেনটা হায়দ্রাবাদ হয়ে আসে, নয়তো ভুবনেশ্বর-পাটনা-রাঁচি হয়ে কলকাতায় যায়, সেই প্লেনে কলকাতা ফিরে যাব।
ভুবনেশ্বর, ওড়িশার রাজধানী। সেখানে অত্যন্ত দক্ষ সব ডাক্তার এবং ভাল ভাল হাসপাতালও আছে কিন্তু আমরা ঋজুদার ব্যাপারে দায়িত্ব নিতে রাজি ছিলাম না। ঋজুদাতো শুধুমাত্র আমার আর তিতির আর ভটকাই-এর ঋজুদা নয়, ঋজুদা জাতীয় সম্পত্তি। তাঁর কিছু একটা হয়ে গেলে, অন্যদের কথা ছেড়েই দিলাম, শ্রীমান ভটকাইচন্দ্র এবং গদাধরদাই আমাদের পিঠের চামড়া খুলে নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।
যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের মালপত্র জিপের সামনের সিটে উঠিয়ে নিয়ে তিতির ঋজুদাকে কোলে শুইয়ে বসল পিছনে। সঙ্গে সামনে মহান্তিবাবুও উঠলেন পট্টনায়েকবাবুর প্রতিভূ হিসাবে। ওঁরা কৃতজ্ঞ যেমন ছিলেন, লজ্জিতও কম ছিলেন না। তারপর স্টিয়ারিং-এ বসে আমি টিকিয়া উড়ান চালালাম জিপ অঙ্গুলের দিকে।
বিমলবাবুর বাড়িতে সিমলিপদাতে এক মিনিট দাঁড়িয়ে বিমলবাবুকে খবরটা দিয়ে যেতে হবে, যাতে উনি বড় হাসপাতালে ওঁর ড্রাইভার এবং অন্য একটা গাড়ি নিয়ে আসেন এক্ষুনি। জিপ তো কারও চালিয়ে ফিরতে হবে ভুবনেশ্বর থেকে!
করতপটার কাছাকাছি এসেই ঋজুদা বলল, আমার শীত করছে রে। আমাদের সঙ্গে একটা করে কম্বল ছিল। তিতির তাই চাপিয়ে দিল ঋজুদার গায়ে। উধ্বাঙ্গের সমস্ত ক্ষত থেকে তখনও রক্ত চোঁয়াচ্ছিল। রক্তক্ষয় হয়েও কিছু না হয়ে যায়। ভাবছিলাম আমি। তা ছাড়া বাঘের নখে ও মুখে তীব্র বিষ থাকে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ক্ষতগুলোতে ‘গ্যাংগ্রিন’ সেট করে যাবে। তখন বাঁচানো মুশকিল। হাত পা হলে তা কেটে বাদ দিয়ে রোগীকে বাঁচানো যায় কিন্তু এ তো বুক, পেট, কাঁধ ও বাহুর সংযোগস্থলের ক্ষত। বাম উরু থেকেও এক খাবলা মাংস উড়িয়ে নিয়েছে নিজে মরতে-বসা বাঘিনী।
করতপটার মানুষরা পথের উপরে জটলা করে দাঁড়িয়েছিল। তারা মহান্তিবাবুকে দেখেই হই হই করে জিপ থামিয়ে ঋজুদাকে মালা পরাল, প্রণাম করল। ছাড়তেই চায় না। মহান্তিবাবু ধমক-ধামক দিয়ে এবং আগামীকাল থেকে তাদের কাজে যোগ দিতে বলে আমাকে বললেন, এবারে জিপ এগোন।
আমি আবার জোরে অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিলাম।
ঋজুদার আচ্ছন্নভাব কাটাবার জন্য মহান্তিবাবু বললেন, বুঝলেন কিনা ঋজুবাবু, আপনার ক্ষত পচে যাবার কোনও দুর্ভাবনাই আর নেই। ভাগ্যিস হাড়িবন্ধু ওখানে এসেছিল। ব্যাটা করে না এমন নেশা নেই। ওকে একবার একটা গোখরো সাপ কামড়ে দিয়েছিল।
তারপর?
তিতির বলল।
তারপর আর কী। সাপটাই হাড়িবন্ধুর শরীরের বিষে ঢলে পড়ল।
ওই টেনশনের মধ্যেও আমি হেসে উঠলাম, বললাম, বলেন কী?
তবে আর কী বলছি। বাঘ বা চিতা যদি কামড়ায় তবে সঙ্গে সঙ্গে যদি সেখানে মুতে দেন তবে অ্যান্টিসেপটিকের কাজ করে। অমন অ্যান্টিসেপটিক খুব কমই আছে।
তিতির হেসে উঠল মহান্তিবাবুর কথায়।
আমার চোখের সামনে বাগানে পাইপে করে জল দেওয়ার মতো ডান হাতে প্রত্যঙ্গটি যত্নভাবে ধরে হাড়িবন্ধুর ঋজুদার সর্বাঙ্গে সেই দুর্গন্ধ জল দেওয়ার ছবিটা ফুটে উঠল। আর জলও কী জল! যেন পি সি সরকারের ‘ওয়াটার অফ ইন্ডিয়া। না আছে আদি, না অন্ত, পড়ছে তো পড়ছেই।
হঠাৎ জড়ানো গলাতে ঋজুদা বলে উঠল, মহান্তিবাবু ঠিকই বলেছেন। এতে কত শিকারি বেঁচে গেছে। হটবাবু খুবই বুদ্ধিমানের কাজ করেছিলেন।
তারপর আমাকে বলল, তুই আফ্রিকান হোয়াইট হান্টার Pondoro-র লেখা পড়িসনি রুদ্র? সেই যে একটা লেপার্ড গুলি খেয়ে গাছের উপর থেকে ওঁর গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে সাংঘাতিকভাবে আহত করল আর তখন তাঁর আফ্রিকান Gun-bearer তাঁর গায়ে ওই কর্ম করে দিয়ে তাঁকে ডিসইনফেক্ট করল!
আমি বললাম, হ্যাঁ হ্যাঁ। মনে পড়েছে। ভুলেই গিয়েছিলাম।
হুঁ। মনে রাখবি। যেখানে সঙ্গে সঙ্গে মেডিক্যাল অ্যাটেনশান পাওয়ার সম্ভাবনা কম সেখানে প্রিভেন্টিভ হিসাবে এই প্রক্রিয়ায় ভিজতে পারলে ভালই।
তিতির হেসে বলল, উঃ মাগো। আমি মরে গেলেও যাব কিন্তু তোমার এই প্রেসক্রিপশনের ওষুধ আমি খাব না।
খাবে কেন? লাগাবেই তো শুধু। আমি বললাম।
খেলেই বা দোষ কী?
ঋজুদা বলল।
তারপর বলল, মোরারজি দেশাই তো নিয়মিত খেতেন। আমি তাঁর পঁচাশি বছর বয়সে তাঁকে কাছ থেকে দেখেছি। কী রং, কী গড়ন, যেন সাহেবের বাচ্চা।
আমি আর ওই মূত্র-তত্ত্বে সামিল হলাম না। মনটা খারাপ লাগছিল। বাঘিনীটার চামড়া ছাড়ানোর সময়ে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখতে হত, কেন সে মানুষ ধরা আরম্ভ করল, কোন দুঃখে?
কোনও দুঃখ বা অসীম অসুবিধা ছাড়া কোনও বাঘই মানুষখেকো হয় না। সুন্দরবনের বাঘের কথা ছাড়া। তারা বংশপরম্পরায় আনন্দের সঙ্গেই মানুষ মেরে আসছে বহু যুগ থেকে। বাঘ বা বাঘিনী যে দুঃখে বা শারীরিক যন্ত্রণার কারণে মানুষখেকো হয়, সেই দুঃখ কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষেরই দেওয়া। এটা আমাদের লজ্জা। নইলে বাঘের মতো মহান, পুরুষ-মানুষের সংজ্ঞা, অকুতোভয়, ভদ্রলোক, জ্ঞানী, পৃথিবীতে নেই। মানুষের অনেকই শেখার ছিল তাদের কাছ থেকে। মানুষ মূর্খ বলে, আত্মম্ভরিতার শিকার বলেই বাঘের কাছ থেকে শিখল না কিছুই।
তিতির বলল, ওরা বোধহয় এখন বাঘকে নিয়ে করতপটাতে আসবে। চামড়া ছাড়াতে দেরি হয়ে গেলে চামড়াটা নষ্ট হয়ে যাবে।
কিছু হবে না। হাড়িবন্ধু আছে, ভীম্ব আছে। ওরা সব বাঘের চামড়া ছাড়াতে ওস্তাদ। পেটের চর্বি, বাঘের নখ, বাঘের গোঁফ এসব তো ওরাই নেবে কিনা! কোনও চিন্তা করবেন না, চামড়া ছাড়িয়ে, নুন আর ফটকিরি দিয়ে ফকিনা কলকাতাতে আপনাদের ঠিকানাতে প্যাক করে পাঠিয়ে দেব।
আমি বললাম, না না, আমাদের কারও ঠিকানাতেই নয়, কলকাতার কার্থবাটসন অ্যান্ড হার্পার অথবা ম্যাড্রাসের ভ্যান ইনজেন অ্যান্ড ভ্যান ইনজেন-এ পাঠাতে হবে। দু’জনের ঠিকানাই আমি আপনাকে দিয়ে যাব।
ঋজুদা ঘোরের মধ্যেই বলল, কবে থেকে চোর হলি তুই রুদ্র?
মানে?
মানে, বাঘটা কি তোর? না আমার?
মহান্তিবাবু বললেন, এ কী কথা। বাঘটাতো আপনারাই মারলেন। আপনাদের নাতো বাঘিনী কার?
ঋজুদা কষ্ট করে হলেও হেসে বলল, বাঘিনী মিস্টার হটবাবুর।
সে কী। সে ব্যাটাই তো তার গাদা বন্দুক হাঁকড়ে বাঘটাকে খণ্ডিয়া করে দিল। খন্ডিয়া না হলে কি আর সে আপনাকে আক্রমণ করত?
খন্ডিয়া মানে কী?
তিতির জিজ্ঞেস করল।
খন্ডিয়া মানে আহত। ইনজিওরড।
ও।
ঋজুদা বলল, সে যাই হোক, বাঘ শিকারের নিয়ম হল, যে বাঘের শরীর থেকে প্রথম রক্তপাত ঘটাবে বাঘ তারই।
এ আবার কী নিয়ম? কোনও আনাড়ি যদি বাঘের ল্যাজে বা পায়ের থাবাতে গুলি করে তবেও সে বাঘ তার?
হ্যাঁ, তার। যে-শিকারি নিজের জীবন বিপন্ন করে সেই সামান্য আহত কিন্তু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ বাঘকে খুঁজে পেতে মারবেন বাঘ তাঁর নয়। যে আনাড়ি প্রথম রক্তপাত ঘটিয়েছে বাঘ তারই।
ভারী অদ্ভুত নিয়ম তো।
সে ষড়া সেই বাঘকু চম লইকি কন করিবে? কুয়ারে রাখিবে? তাংকু ড্রয়িংরুম অছি না আউ কিছি। আমিই ওটা নিয়ে নেব।
ঋজুদা বলল, আপনার ক’জন শালি মহান্তিবাবু।
তা ভগবানের দয়াতে কম নয়। ছ’জন শালি আমার।
তবে আর কী? ছয় শালিকে রোমহর্ষক মানুষখেকো বাঘ শিকারের গল্পও শোনাতে পারবেন এবং ওই কল্পিত ভয়াবহ কাহিনী শুনে শালিরা আপনার বীরত্বে গা ঘেঁষে বসে বলবে, বাপ্পালো বাপ্পা। উঁইবাবু আপনংকু এত্বে সাহস!
চাইকি কোনও শালী চুমুও খেয়ে দিতে পারে।
আমরা এবং মহান্তিবাবু নিজেও হেসে উঠলেন ঋজুদার কথাতে। তারপর উনি সখেদে বললেন, দুঃখের কথা কী বলব আমার স্ত্রীই সবচেয়ে ছোট বোন। সবচেয়ে বড় শালির বয়স সাতাশি আর আমার স্ত্রীর উপরে যিনি তাঁর বয়স পঁয়ষট্টি। সিনিয়র সিটিজেন। অর্ধেক ভাড়াতে ট্রেনে যাতায়াত করেন। সকলেই কি আর শালিবাহন হয় ঋজুবাবু? সে সব কপালের ব্যাপার!
ঋজুদা হেসে ফেলল রসিক মহান্তিবাবুর কথা শুনে।
অঙ্গুলে পৌঁছে কোনও দোকানে হুইস্কি পাওয়া যায় কি না দেখিস তো রুদ্র।
তুমি তো ওসব খাওনা।
খাইতো নাই। সেই জন্যই এখন খেলে ওষুধের কাজ দেবে। এখানে তো স্কচ পাবি না, রয়্যাল চ্যালেঞ্জ অথবা পিটার স্কট বা ওকেন-গ্লো যাই পাস তাই নিবি। Shock কেটে যাবে। মৃত্যুর হাত থেকেই তো বেঁচে এলাম।
মহান্তিবাবু দার্শনিকের মতো বললেন, জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে তফাত তো এক চুলের। জন্মের পর থেকেই তো মৃত্যুর হাতে হাত রেখেই আমাদের চলা। আপনি তো তাও বাঘিনীকে গুলি করে জখম হলেন, যুধিষ্ঠির যে হিসি করতে গিয়ে অতর্কিতে অক্কা পেল। আর মৃত্যু কী রকম! ভয়াবহ! ওর আত্মা কি আর মুক্ত হবে? সে নিশ্চয়ই বাঘডুম্বা হয়ে যাবে।
বাঘডুম্বা আবার কী জিনিস?
বাঘডুম্বার নাম শোনেননি?
নাতো। সে কি বাঘমুণ্ডার কোনও জানোয়ার?
মহান্তিবাবু বললেন, বাঘঘডুম্বার সঙ্গে বাঘমুন্ডার কোনও সম্পর্ক নেই। যেসব মানুষে বাঘের হাতে মরে, তারা এক রকমের স্পেশ্যাল ভূত হয়ে যায়। পাখির রূপ ধরে তারা রাতের বেলা ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে ডেকে ওঠে কিরি-কিরি কিরি-কিরি, ধ্রুপ-ধুপ-ধ্রুপ-ধ্রুপ। ওড়িশার কালাহান্ডিতে অনেক বাঘঘডুম্বা আছে। কারণ, সেখানে প্রায় সব বাঘই মানুষখেকো। বাঘমুন্ডার জঙ্গলেও আছে।
কী করে জানলেন?
ঋজুদা জিজ্ঞেস করল।
আমি একবার বিকেল-বিকেল ট্রাক ড্রাইভারের মুখে আমার স্ত্রীর ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া হয়েছে খবর পেয়ে পট্টনায়েকবাবুর জিপ নিয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে রাতের বেলা ঢেনকানলে যাচ্ছিলাম। এইট্টি সেভেনের এপ্রিল মাসে। বাঘমুন্ডার জঙ্গলে রাতে ট্রাক ড্রাইভাররাও হাতির ভয়ে ট্রাক চালায় না। দিনের আলো থাকতে থাকতে আসে আবার দিনের আলো ফুটলেই রওনা দেয় কটকের দিকে। বাঘমুন্ডা বন-বাংলোর কাছেই আমাদের ক্যাম্প পড়েছিল সেবারে। বাংলোর হাতাতে যে কুয়ো আছে, সেখান থেকেই খাবার জল আসত আমাদের, চান, কাপড় কাঁচা সবই ওই কুয়োতেই হত। ক্যাম্প থেকে গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে জিপ চলছে, গরমের দিন, জঙ্গল ফাঁকা ফাঁকা হয়ে গেছে, আগাছা একেবারেই নেই। একটা বাঁক নিয়েছিল রাস্তাটা। প্রায় সমকৌণিক বাঁক। এবং সেই বাঁকের মুখেই হাতির দলের সঙ্গে মোলাকাত হয় বলে ড্রাইভার অমরিক সিং খুব সাবধানে বাঁকটা ঘুরল গতি কমিয়ে যাতে হাতির পেটে গিয়ে গুঁতো না মারে। কিন্তু বাঁক নিতেই দেখি হাতি-টাতি নেই। পথের উপরে নাইটজার পাখির একজোড়া চোখ লাল আগুনের গোলার মতো দপ করে জ্বলে উঠল। ওই পাখিগুলো শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ওড়ে না, জিপ যখন তাদের ঘাড়ে গিয়ে পড়ে তখন সোজা উপরে উঠে যায়, এমনভাবে যায়, যেন মনে হয় বনেট ফুড়েই উঠল। পাখিটা উড়ে ওঠামাত্রই বাঁপাশের একটি মিটকুনিয়া গাছের ঝাঁকড়া ডালের আড়াল থেকে বাঘঘডুম্বা ডেকে উঠল কিরি-কিরি-কিরি-কিরি, ধূপ-ধূপ-ধূপ-ধ্বপ! সেই ডাক শুনে তো আমাদের পিলে চমকে গেল। এর চেয়ে হাতির দলের গায়ে ধাক্কা মারাও কম বিপজ্জনক ছিল।
অমরিক সিং-এর এমনিতে দুর্জয় সাহস। একবার জ্বলন্ত চেলা কাঠ নিয়ে সে একটা বড় বাঘকে তাড়া করে গিয়েছিল। বাঘটা কাঠ ঢোলাইওয়ালাদের মোষ ধরবার জন্য ক্যাম্পের কাছে ঘুর ঘুর করছিল যখন সন্ধে রাত্তিরে। কিন্তু দুঃসাহসী অমরিক সিং-এর সবরকম ভূতের ভয় ছিল। রাজ্যের কুসংস্কার ছিল। শিয়াল জিপের সামনে দিয়ে পথের বাঁদিক থেকে ডানদিকে গেলে, খরগোশ ডানদিক থেকে বাঁদিকে গেলে সে জিপ থামিয়ে গ্রন্থসাহেব থেকে মন্ত্র আওড়াত ভক্তিভরে বেশ কিছুক্ষণ পরেই আবার মন্ত্রপড়া শেষ হলে তারপরই জিপের অ্যাকসিলারেটরে কষে চাপ দিত। ভূত বলে ভূত। বাঘঘডুম্বা ভূত। অমরিক সিং যে কী জোরে জিপ ছুটিয়েছিল সে রাতে তা কী বলব! গিয়ার বদলাতে পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিল ভয়ের চোটে। পুরো পথটাই সেকেন্ড গিয়ারে এল জিপ গাঁক গাঁক করতে করতে। বনেটের নীচ থেকে ধোঁয়া বেরোতে লাগল। আমি ভাবলাম বুঝি আগুনই লেগে যাবে জিপে। তারপর বড় রাস্তাতে পড়ে এক চাষার বাড়ির পুকুর থেকে অনেক বালতি জল জিপের গায়ে মাথায় এবং রেডিয়েটরে ঢেলে তবেই জিপকে ঠাণ্ডা করা হয়–আর একটু গেলে সত্যি সত্যিই আগুন লেগে যেত। রেডিয়েটরে জল ছিল না এক ফোঁটাও। তাই বলছিলাম, বাঘডুম্বা নিয়ে স্যার ঠাট্টা করবেন না। অমন সাংঘাতিক ভূত ইন্ডিয়ার আর কোথাও নেই।
তিতির টিপ্পনী কেটে বলল, অমরিক সিং-এর কথা তো বললেন, আপনি ভয় পেয়েছিলেন কি না তা তো বললেন না?
মহান্তিবাবু হাসলেন। বললেন, ভয় কি আর পাইনি ম্যাডাম। ভয়ের চোটে দাঁতকপাটি লেগে গিয়েছিল কিন্তু আমি যে মুহুরি, ম্যানেজার। আমিও যদি ভয় পাই তাহলে তো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন লাটে উঠবে। এই বাঘডুম্বা ভূতের কথা ছেড়ে দিন, বাঘডুম্বার বাঘের ভয়ও কি পাইনি! দু রাতে বাঘটা ক্যাম্পে আমার ঘরের সামনে এসেছিল।
সে তো আপনার গড়গড়া থেকে তামাক খেতে।
আমি বললাম, গিয়ার চেঞ্জ করতে করতে।
মহান্তিবাবু হেসে ফেললেন। বললেন, তা হতেও বা পারে। কিন্তু সাতসকালে উঠে তার পায়ের দাগ আমার ঘরের সামনে দেখে আমি নিজেই পা দিয়ে মুছে দিয়েছিলাম, যাতে কেউ টের না পায়। যা বলার, তা আমি শুধু বাবুকেই রিপোর্ট করতাম। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালানো কি সোজা কথা! টাটা কোম্পানিও কোম্পানি, আমাদের পট্টনায়েক অ্যান্ড কোম্পানিও কোম্পানি। তফাত বিশেষ নেই। রুসি মোদিও যা, আমিও তাই।
দেখতে দেখতে আমরা অঙ্গুলে পৌঁছে সিমলিপদাতে বিমলকান্তি ঘোষের বাড়ি পৌঁছে গেলাম। উনি আগেই খবর পেয়েছিলেন। পুরুণাকোট পুলিশ চৌকি থেকে অঙ্গুলের বড় থানাতে ওয়্যারলেস করে দিয়েছিল। থানা থেকে বিমলবাবুকে ফোনে খবর দিয়ে রেখেছিল। বিমলবাবু বাদাম দেওয়া, ধনেপাতা দেওয়া, চিড়ে ভাজা, আর বড় বড় পিস-এর রুই মাছ ভাজা খাওয়ালেন পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই আদর করে। বিমলবাবুর স্ত্রীর রান্নার হাতই আলাদা।
ঋজুদা বলল, কত যে অত্যাচার করেছি বউদির উপরে একসময়ে আমরা। আমরা চাও খেলাম। উনি ঋজুদার জন্য এক বোতল হোয়াইট লেবেল স্কচ হুইস্কি দিয়ে দিলেন। বললেন, খেতে খেতে ভুবনেশ্বরে চলে যান। চাঙ্গা লাগবে। বহু বছর আগে গুহসাহেব শিকারে এসে দিয়ে গেছিলেন। রাখা ছিল। আমি তো জন্মে জল, চা, সরবৎ আর ঢাকার আয়ুর্বেদিক ঔষধালয়ের সারিবাদি সালসা’ ছাড়া অন্য কোনও তরল পদার্থই খাইনি। তবে প্রায় চল্লিশ বছর আগে টিটাগড় পেপার মিলের উইলিস সাহেব টুকার জঙ্গলে বাঘের মুখে পড়ে সাংঘাতিকভাবে আহত হওয়ার পর তাঁকে দেখেছিলাম স্কচ-এর বোতল খুলে নীট-হুঁইস্কি বোতল থেকে খেতে। কটক অবধি যেতে যেতে মরে যে যাননি তাও ওই হুইস্কির জন্য, ডা. প্রধান আমাকে বলেছিলেন কটকে। সেই দিনই বুঝেছিলাম এ জিনিস মৃতসঞ্জীবনী। তবে নিজের কখনও খাওয়ার প্রয়োজন হয়নি। তাই গুহ সাহেবের প্রেজেন্ট করা ভালবাসার দান রেখে দিয়েছিলাম যত্ন করে। এমন সৎকাজে লাগবে আগে জানিনি। ঋজুবাবু আমার খুবই ভালবাসার জন। তাঁকে আমি একাধিক কারণে শ্রদ্ধাও করি।
ওই। শুরু করলেন। বোতলটা দিন তো বক্তৃতা থামিয়ে।
জিপটাকে আমি বিমলবাবুর বাড়ির সামনের মস্ত তেঁতুল গাছটার ছায়াতে রেখেছিলাম। ঋজুদার জিপ থেকে নামার মতো অবস্থা ছিল না।
জিপে বসেই চিড়ে ভাজা আর মাছ ভাজা খেল। ঋজুদার মুখের হাসি কিন্তু নেভেনি। অনির্বাণ। ঋজুদা চা না খেয়ে হুইস্কি খেল বোতল থেকে স্ট্রেট দু’চুমুক। স্বীকার করছে না বটে কিন্তু বেশ ঘোরে আছে। তিতির কপালে হাত দিয়ে দেখল, জ্বরও এসেছে।
বিমলবাবু বললেন, এবারে খুব জোরে চালিয়ে চলে যাও রুদ্র। আর দেরি কোরো না। ডা. পানিগ্রাহীকে বলে দিয়েছি। উনি আজ বাড়িতে খেতে যাবেন না। চেম্বারেই থাকবেন। চেম্বার ভুবনেশ্বরে ঢোকার মুখেই পড়বে। সঙ্গে নার্সিং হোমও আছে। সব বন্দোবস্ত করা আছে। হাইওয়ের উপরেই পড়বে। প্লেনের টিকিটও উনি কিনে রেখেছেন। আমি একটু পরেই রওনা হচ্ছি খেয়ে-দেয়ে, আমার ড্রাইভারকে সঙ্গে নিয়ে। বড় গাড়ি থাকলে ঋজুবাবুকে তাতেই ট্রানসফার করে দিতাম। মারুতি এইট হান্ড্রেড তো! আমি সোজা এয়ারপোর্টে যাব। ড্রাইভার জিপ চালিয়ে ফিরে আসবে ফ্লাইট টেক-অফ করার পরে। আর আমি গাড়ি নিয়ে ফিরব মহান্তিবাবুকে সঙ্গে নিয়ে। ফেরার পথে ঢেনকানল-এ তাঁকে নামিয়েও দিয়ে যাব।
আপনারা নার্সিং হোমের থেকে ফ্লাইটের সময় বুঝে রওনা হবেন এয়ারপোর্টের দিকে। হুইল চেয়ারের বন্দোবস্ত আমি করে রাখব আগেই। এয়ারপোর্ট ম্যানেজারকেও বলে রাখব।
বাড়িতে না নামিয়ে পট্টনায়েকবাবুর বাড়িতেই নামাবেন বরং।
যুধিষ্ঠিরটা চলে গেল।
মহান্তিবাবু বললেন।
ওঃ তাই তো। আমরাও তো একবার যাওয়া উচিত। বিমলবাবু বললেন। এত বড় সর্বনাশ হয়ে গেল ভদ্রলোকের। যুধিষ্ঠির ছেলেটা বড়ই ভাল ছিল। বিনয়ী, ভদ্র। বড়লোক বলে কোনও চাল-চালিয়াতি ছিল না। অন্য অনেক বড়লোকের ছেলেদের মতো। পান-সিগারেট পর্যন্ত খেত না। সুন্দর স্বভাব।
মহান্তিবাবু বললেন, ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন বিমলবাবু। আপনার গড়গড়াটা আনতে বলুন তো জগবন্ধুকে, তাম্বুরি তামাক সেজে। বড় বড় দুটান লাগিয়েই ‘জয় মা কটকচণ্ডী: বলে ভুবনেশ্বর রওনা দিই।
তারপর বললেন, শুনেছেন নাকি সে কথা? হটবাবু বলছিলেন বাঘিনীটা নাকি ক্যাম্পে ঢুকেছিলই আমার সুগন্ধি তামাক সাজা গড়গড়াতে দু’টান লাগাবে বলে।
আমরা সকলেই হেসে উঠলাম।
মহান্তিবাবু গড়গড়াতে গুড়ুক গুড়ুক করে কয়েক টান লাগানোর পরে, বিমলবাবু বললেন, আর দেরি নয়। এগোন। এখোন।
পেইনকিলার ট্যাবলেট কিছু কি দিয়ে দেব?
ঋজুদা হোয়াইট লেবেল-এর বোতলটা দেখিয়ে বলল, এই তো নিজৌষধি দিলেন। সর্বরোগহারী। আর কিছুই লাগবে না।
তারপর বলল, এবারে এদের কিছুই দেখাতে পারলাম না। শীত থাকতে থাকতেই আর একবার আসার ইচ্ছে আছে। তবে আমি কখন কোথায় থাকি, তা নিজেই জানি না। নিজে না আসতে পারলে এদের আপনার হেপাজতেই পাঠিয়ে দেব। ভাল করে সাতকোশীয়া গন্ড ঘুরিয়ে দেবেন।
পাঠাবেন। দেখিয়ে দেব। নিশ্চয়ই দেব। তবে আপনি এলে মজাই আলাদা। চেষ্টা করবেন আসবার অবশ্যই।
আমরা বিমলবাবুকে হাত নেড়ে এগোলাম। সিমলিপদা থেকে বড় রাস্তায় পড়েই অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিলাম। তবে জিপে আশি কিলোমিটারের চেয়ে জোরে যানবাহন ভরা পথে যাওয়া বিপজ্জনক। এক বিপদ থেকে বেঁচে অন্য বিপদে না পড়ি।
ঋজুদা বলল, জিপটা বাঁদিকে করে একটু আস্তে কর রুদ্র। পাইপটা ধরাব।
ধরাও। বলে আমি অ্যাকসিলারেটর ছেড়ে দিয়ে সটাসট করে গিয়ার চেঞ্জ করে গতি কমালাম। বললাম, ভাল করে ধরাও তো। আর থামাথামি নেই। তিতিরের কাঁধে হেলান দিয়ে এবার একটু ঘুমিয়ে পড়ো৷
একদম না।
মহান্তিবাবু বললেন। চোখের পাতা একেবারে এক করবেন না। গল্প করতে করতে চলুন।
ঋজুদা বলল মহান্তিবাবুকে, রাইট ইউ আর।
তারপর আমাকে বলল, আফ্রিকার গুগুনোগুম্বারের দেশের কথা মনে পড়ে রুদ্র? সেই সেরেঙ্গেটি প্লেইনস-এ ভুষুন্ডার বিশ্বাসঘাতকতার কথা?
আদিগন্ত ঘাসবনে পথ হারাবার কথা? হায়নাদের আক্রমণের কথা। তুই যে কতবার আমাকে কতভাবে বাঁচাবি রুদ্র, তুই-ই হচ্ছিস আমার বিপদে মধুসূদন।
তিতির বলল, ‘গুগুনোগুম্বারের দেশে’ বইটাও তুমি দারুণ লিখেছিলে রুদ্র।
তারপর আর কথা না বলে, জিপ চালাতে চালাতে আমি ভাবছিলাম, যুধিষ্ঠিরের অমন মর্মান্তিক মৃত্যু না হলে আমরা এতক্ষণে মহানদী পেরিয়ে, মানে মহানদীর গণ্ড পেরিয়ে কোথায় না কোথায় চলে যেতাম। বৌধ, নয়তো ফুলবানীতে। ফুলবানী অনেক উঁচু জায়গা। নয়তো চারছক হয়ে দশপাল্লা। যেখানে টাকরা গ্রামে পৌঁছে বুরতং নালাকে ডানপাশে রেখে, চলে যেতাম সুউচ্চ বিরিগড় পাহাড়শ্রেণীর নীচের ছোট্ট গ্রাম বুরুসাইতে। সেখান থেকে পাহাড়ে চড়তাম। এই সব অঞ্চলে খন্দ উপজাতিদের বাস–যাদের পূর্বপুরুষরা মেঘের ভেলাতে চড়ে এসে ওই সুউচ্চ পাহাড়ে নেমে বসতি স্থাপন করেছিল।
যখনই আমার মন খারাপ হয়, আমি রুদ্র রায়, নিজেই নিজের লেখা ‘ঋজুদা সমগ্র’র পাতা খুলে বসে পড়ি। আর কোথায় না কোথায় চলে যাই। কত কথাই যে মনের কোণে ভেসে ওঠে। ভাগ্যিস ঋজুদা ছিল আমাদের!