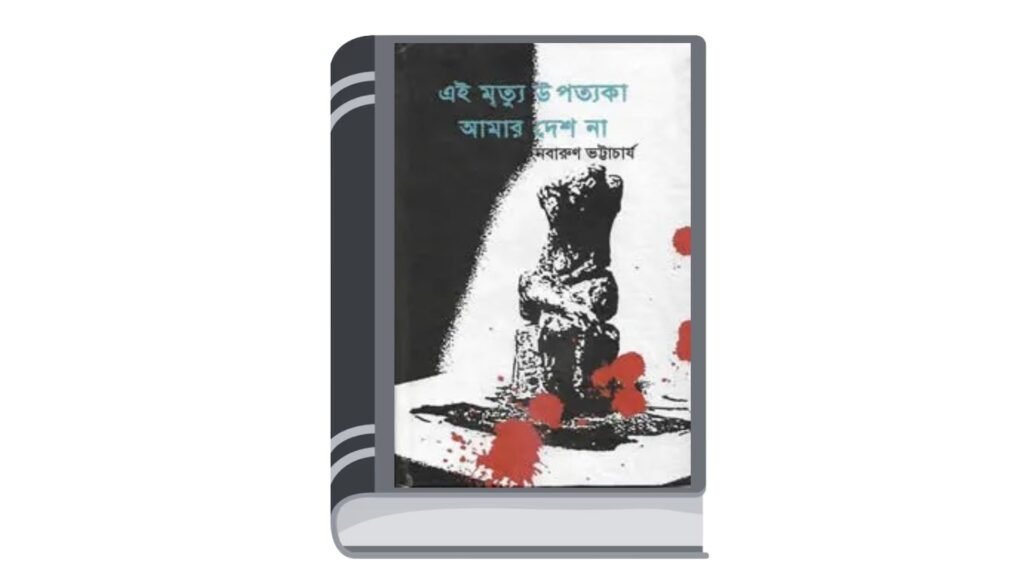কে?
কে?
পনেরই সেপ্টেম্বর 1945।
অর্থাৎ বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে মাত্র একমাস আগে। ইউরেনিয়াম-বোমা-বিধ্বস্ত হিরোশিমা আর প্লুটোনিয়াম-বোমা-বিধস্ত নাগাসাকির ধ্বংসস্তূপ তখনও সরানো যায়নি। জার্মানি, রাশিয়া, ফ্রান্স অথবা জাপানের অধিকাংশ জনপদ মৃত্যুপুরীতে রূপান্তরিত। বিশ্ব এক মহাশ্মশান! মানব সভ্যতার ইতিহাসে এ পৃথিবীতে এতবড় ক্ষয়ক্ষতি আর কখনও হয়নি। সেই মহাশ্মশানে শুধু শোনা যায় মিত্রপক্ষের বিজয়োল্লাসের উৎসব-ধ্বনি–যেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানে মাংসভুক শিবাকুলের উচ্ছ্বাস!
প্রিয়-পরিজনদের নিয়ে প্রাতরাশে বসেছিলেন অশীতিপর বৃদ্ধ স্টিমসন। ওয়াশিংটনের অনতিদূরে হাইহোল্ডে, তার বাড়ির ‘ডাইনিং হল’-এ। অশীতিপর ঠিক নন, হেনরি. এল. স্টিমসনের বয়স ঊনআশি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবীণ সমরসচিব সেক্রেটারি অফ ওয়্যর। এ বিশ্বযুদ্ধে ছিলেন আমেরিকার সর্বময় কর্তা। প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের আমলের লোক–এই বয়সেও অবসর নেননি কর্মজীবন থেকে। নেবার সুযোগও হয়নি। তাকে এতদিন অব্যাহতি দিয়ে উঠতে পারেননি রুজভেল্টের স্থলাভিষিক্ত নতুন প্রেসিডেন্ট-হ্যারি ট্রুম্যান। অন্তত যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত।
তা সেই যুদ্ধ এতদিনে শেষ হল। এবার ছুটি দাবী করতে পারেন বটে স্টিমসন। বিবদমান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একমাত্র আমেরিকার ভূখণ্ডে কোনো লড়াই হয়নি ক্ষতি হয়েছেপ্রচণ্ড ক্ষতি–আর্থিক এবং জনবলে; কিন্তু আমেরিকার মাটিতে কোনো রক্তপাত ঘটেনি। এজন্য নিশ্চয় অভিনন্দন দাবী করতে পারেন যুদ্ধসচিব। শুধু তাই বা কেন? এ-যুদ্ধের যা চরম ডিভিডেন্ড–আগামী বিশ্বযুদ্ধে তুরুপের টেক্কা-সেটা খেলার শেষে রয়ে গেছে তারই আস্তিনের তলায়! এটা যে কতবড় প্রাপ্তি তা শুধু তিনিই জানেন; আর বোধকরি জানেন–মহাকাল!
হঠাৎ ঝঝন্ করে বেজে উঠল টেলিফোনটা। স্টিমসন মুখ তুলে তাকালেন না। ছুরি-কাটায় যেমন ছিলেন তেমনিই ব্যস্ত রইলেন। টেনে নিলেন জোড়া পোচ-এর প্লেটটা। আবার কোথাও বিজয়োৎসবের আমন্ত্রণ হবে হয়তো! এখন ওই তো দাঁড়িয়েছে একমাত্র কাজ! অর্কেস্ট্রা-নাচ-টোস্ট আর পারস্পরিক পৃষ্ঠ-কণ্ডুয়ন কমপ্লিমেন্টস্ আর কথ্রাচুলেশ। ওঁর নাতনি উঠে গিয়ে টেলিফোনটা ধরল, জানালো গৃহস্বামী প্রাতরাশে ব্যস্ত। পরমূহূর্তেই চমকে উঠল মেয়েটি। টেলিফোনের ‘কথা-মুখে’ হাত চাপা দিয়ে ফিসফিসিয়ে ওঠে : গ্র্যান্ড-পা! ইটস্ ফ্রম হিম্।
হিম! ছুরি-কাঁটা নামিয়ে রাখলেন স্টিমসন। এতে সর্বনামের সার্বজনীন ‘হিম’ নয়, এ আহ্বানে লেগে আছে হোয়াইট-হাউসের হিমশীতল স্পর্শ! টেলিফোনের সঙ্গে যুক্ত ছিল অনেকখানি বৈদ্যুতিক তার–তাই পর্বর্তকেই এগিয়ে আসতে হল মহম্মদের কাছে। যুদ্ধসচিবকে আর উঠে যেতে হল না। ন্যাপকিনে মুখটা মুছে নিয়ে যন্ত্রবিবরে শুধু বললেন : স্টিমসন।
-আপনাকে প্রাতরাশের মাঝখানে বিরক্ত করলাম বলে দুঃখিত। একবার দেখা হওয়া দরকার। আসতে পারবেন?
–শ্যিওর! বলুন কখন আপনার সময় হবে?
–এখনই!
–এখনই! কিন্তু কী ব্যাপার বলুন তো…মানে, এখনই আসছি আমি।
–ধন্যবাদ!-লাইন কেটে দিলেন হ্যারি ট্রুম্যান।
পিতার বয়সী প্রবীণ রাজনীতিককে প্রেসিডেন্ট বরাবরই যথেষ্ট সম্মান দেখিয়ে এসেছেন। তাহলে এভাবে কথার মাঝখানে কেন লাইন কেটে দিলেন উনি? লৌহমানব পোড়খাওয়া স্টিমসন বুঝতে পারেন–ব্যাপারটা জরুরি, অত্যন্ত জরুরি। না হলে এতটা বিচলিত শোনাতো না প্রেসিডেন্টের কণ্ঠস্বর। কিন্তু কী হতে পারে? রণক্লান্ত পৃথিবীতে আজ এখন এমন কী ঘটনা ঘটতে পারে যাতে অ্যাটম-বোমার একচ্ছত্র অধিকারী আমেরিকার প্রেসিডেন্টের গলা কাপবে? কী এমন দুঃসংবাদ আসতে পারে যাতে বিজয়ী যুদ্ধসচিবকে অর্ধভুক্ত প্রাতরাশের টেবিল ছেড়ে উঠে যেতে হয়?
***
সেই পরিচিত কক্ষ। পরিচিত পরিবেশ। সামনের ওই গদি-আঁটা চেয়ারখানায় ট্রুম্যানের পূর্ববর্তী রুজভেল্টকেই শুধু নয়, আরও অনেক অনেককে ওভাবে বসতে দেখেছেন প্রবীণ স্টিমসন–এমনকি প্রথম যৌবনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অন্তে উড়রো উইলসনকেও!
ঘরে তৃতীয় ব্যক্তি নেই। প্রেসিডেন্ট সৌজন্যসূচক সম্ভাষণের ধার দিয়েও গেলেন না। হয়তো প্রভাতটা আজ সু-প্রযুক্ত মনে হয়নি তার কাছে। মনে হল তিনি রীতিমত উত্তেজিত। স্টিমসন তার চেয়ারে ভাল করে গুছিয়ে বসবার আগেই প্রেসিডেন্ট বলে ওঠেন, মিস্টার সেক্রেটারি! আপনি গোয়েন্দা গল্প পড়েন? কোনান ডয়েল, আগাথা ক্রিস্টি?
স্টিমসন নির্বাক!
হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন ট্রুম্যান। নীরবে পদচারণা শুরু করেন ঘরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে। স্টিমসন যেন পিংপং খেলা দেখছেন। একবার এদিকে ফেরেন, একবার ওদিকে। হঠাৎ পদচারণায় ক্ষান্ত দিয়ে প্রেসিডেন্ট বলে ওঠেন, আজ সকালে কানাডার রাষ্ট্রদূত আমাকে একখানি চিঠি দিয়ে গেছে। প্রাইম মিনিস্টার ম্যাকেঞ্জি কিং-এর ব্যক্তিগত পত্র। আমি…আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি সেখানা পড়ে….
স্তম্ভিত হয়ে গেলেন স্টিমসনও। সম্পূর্ণ অন্য কারণে। তিনি মনে মনে। ভাবছিলেন–হ্যায় ঈশ্বর! স্তালিন নয়, চার্চিল নয়–শেষ পর্যন্ত ম্যাকেঞ্জি কিং! তাতেই এই রণক্লান্ত দুনিয়ার একচ্ছত্র অধীশ্বর হ্যারি ট্রুম্যান এতটা বিচলিত।
প্রেসিডেন্ট নিজ আসনে এসে বসলেন। বললেন, আপনি অবসর চাইছিলেন; কিন্তু এ ব্যাপারটার ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত…।
-কিন্তু ব্যাপারটা কী? কী লিখেছেন প্রাইম মিনিস্টার ম্যাকেঞ্জি কিং?
–একটা গোয়েন্দা গল্প। অসমাপ্ত কাহিনি! এ শতাব্দীর সবচেয়ে রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা কাহিনির প্রথমার্ধ!
সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন মেলোড্রামাটিক লাগল বাস্তববাদী স্টিমসনের কাছে। বললেন, দেখি চিঠিখানা?
ট্রুম্যান টেবিলের উপর থেকে সিলমোহরাঙ্কিত একটি ভারি খাম তুলে নিলেন। বাড়িয়ে ধরলেন স্টিমসনের দিকে। বললেন, ম্যানহাটান-প্রজেক্টের গোপনতম তথ্য ওরা বার করে নিয়ে গেছে!
স্টিমসন স্তম্ভিত! অস্ফুটে বলেন : মানে?
-ইয়েস, মিস্টার সেক্রেটারি! এতক্ষণে মস্কোর বৈজ্ঞানিকেরা তা নিয়ে হাতে-কলমে পরীক্ষা করছেন।
বলিরেখাঙ্কিত উদ্যত হাতটা ধীরে ধীরে নেমে এল স্টিমসনের। একটু ঝুঁকে পড়লেন সামনের দিকে। যেন এইমাত্র একটা 22 মাপের সিসের গোলকে বিদ্ধ হয়েছে বৃদ্ধের পাঁজরা। ককিয়ে ওঠেন তিনিঃ বাটু হাউ অন আর্থ কুড ম্যাকেঞ্জি কিং নো ইট?
ইন্টারকমটাও আর্তনাদ করে উঠল। প্রেসিডেন্টের একান্ত-সচিব নিশ্চয় কোন জরুরি সংবাদ জানাতে চান। কিন্তু ক্ৰক্ষেপ করলেন না ট্রুম্যান। পুনরায় বাড়িয়ে ধরলেন মোটা খামটা। বললেন, এটা পড়লেই বুঝবেন। নিন ধরুন!
আদেশটা বোধহয় কানে যায়নি স্টিমসনের। গভীর চিন্তার মধ্যে ডুবে গেছেন তিনি। কপালে জেগেছে কুঞ্চন। খোলা জানলা দিয়ে দৃষ্টি চলে গেছে বহুদূরে। প্রেসিডেন্ট পুনরায় বলেন : ইয়ে, মিস্টার সেক্রেটারি! দিস্ অসো রিকোয়ার্স এ্যাকশন!
‘অলসো’! অর্থাৎ ইঙ্গিতে প্রেসিডেন্ট বুঝিয়ে দিলেন-এ কোনো যুগান্তকারী উক্তি নয়, ঐতিহাসিক উদ্ধৃতিমাত্র! আর যে-ই ভুলে যাক, যুদ্ধসচিব স্টিমসন ভুলতে পারেন না ওই উদ্ধৃতিটা। ঠিক ওই চেয়ারে বসে আমেরিকার আর এক প্রেসিডেন্ট ঠিক ওই কথা-কটাই বলেছিলেন একদিন। 1939 সালের এগারোই অক্টোবর। সেদিনও মার্কিন প্রেসিডেন্টের হাতে ছিল এমনি একটা ভারি খাম। সেবার সে পত্রখানি এসেছিল লঙ-আইল্যান্ডে পরবাসী শুভ্রকেশ এক বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকের কাছ থেকে। স্থান আর কালের পজিটিভ-ক্যাটালিস্ট সেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকটি সেদিন মার্কিন রাষ্ট্রপ্রধানকে সংকেত পাঠিয়েছিলেন : ‘ইউরেনিয়াম পরমাণুর কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করার মহাসন্ধিক্ষণ সমুপস্থিত। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট সেই চিঠিখানি ঠিক এমন ভঙ্গিতে বাড়িয়ে ধরেছিলেন তার মিলিটারী এ্যাটাশে জেনারেল ‘পা’ ওয়াটসনের দিকে। অতি সংক্ষেপে শুধু বলেছিলেন : পা! দিস্ রিকোয়্যার্স এ্যাকশান।
আজ ছয় বছর পরে সেই ঐতিহাসিক বাক্যটিরই পুনরুক্তি করলেন রুজভেল্টের উত্তরসূরি হ্যারি ট্রুম্যান। তাই ওই ‘অসো। সেবার নির্দেশ ছিল সমুদ্রমন্থনের। সুরাসুরের মন্থনে সমুদ্র মথিত হয়েছিল যথারীতি। তাই আজ আমেরিকা বিশ্বাস। এবার আদেশ হল সেই সমুদ্রমন্থনে উঠে আসা-না অমৃতভাণ্ড নয়, হলাহল-অপহারককে খুঁজে বার করতে হবে।
অশীতিপর রণক্লান্ত যুদ্ধসচিব তার বলিরেখাঙ্কিত হাতটি বাড়িয়ে দিলেন। এবার। গ্রহণ করলেন এই দায়িত্ব।
***
ওইদিনই। ঘণ্টাচারেক পরে। ওয়্যর অফিসের সামনে এসে দাঁড়াল ছোট্ট একটা সিট্রন গাড়ি। পার্কিং জোনে গাড়িটি রেখে শিস দিতে দিতে নেমে আসে তার একক চালক। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের একজন মার্কিন সামরিক অফিসার-কর্নেল প্যাশ। বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল চেহারা। সুগঠিত শরীর। দেখলেই মনে হয় জীবনে সাফল্যের সন্ধান সে পেয়েছে এই বয়সেই। তা সে সত্যই পেয়েছে। এফ.বি. আই.-য়ের একজন অতি দক্ষ অফিসার। পদমর্যাদায় প্রথম শ্রেণির নয় তা বলে। কর্নেল প্যাশ ইতিপূর্বে বহুবার এসেছে ওয়্যর অফিসে, যুদ্ধ চলাকালে। নানান ধান্দায়। কিন্তু স্বয়ং যুদ্ধসচিবের কাছ থেকে এমন সরাসরি আহ্বান সে জীবনে কখনও পায়নি। পাওয়ার কথাও নয়। যুদ্ধসচিব এবং কর্নেল প্যাশ-এর মাঝখানে চার-পাঁচটি ধাপ। ওর ‘বস’ কর্নেল ল্যান্সডেলকেই কখনও যুদ্ধসচিবের মুখোমুখি হতে হয়নি। ওয়্যর-সেক্রেটারির অধীনে আছেন চিফ-অফ-স্টাফ জেনারেল জর্জ মার্শাল। প্রয়োজনে বরং তিনিই ডেকে পাঠাতেন এফ. বি. আই.-য়ের প্রধান কর্মকর্তাকে, অর্থাৎ কর্নেল ল্যান্সডেল-এর ‘বস’কে। তার নামটা আজও জানে না প্যাশ। চোখেও দেখেনি কোনোদিন। ঈশ্বরকে যেমন চোখে দেখা যায় না, এক-এক দেশে তার এক-এক অভিধা–এফ. বি. আই.-য়ের প্রধান কর্মকর্তাও যেন অনেকটা সেইরকম। সবাই জানে তিনি আছেন। ব্যস, ওইটুকুই। এভাবেই যুদ্ধমন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষিত হত গোয়েন্দাবাহিনীর। আজ স্বয়ং যুদ্ধসচিবের এডিকং ওকে টেলিফোন করায় তাই একটু বিচলিত হয়ে পড়েছিল কর্নেল প্যাশ। ব্যস্ত হয়ে বলেছিল, আপনি ঠিক শুনেছেন তো? আমাকেই যেতে বলেছেন? ব্যক্তিগতভাবে?
-হ্যাঁ, আপনাকেই। ঠিক দুটোর সময়।
–যুদ্ধসচিব নিজে ডেকেছেন?
–হ্যাঁ, আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না?
কর্নেল প্যাশ তৎক্ষণাৎ টেলিফোন করেছিল তার উপরওয়ালার কাছে; কিন্তু কর্নেল ল্যান্সডেলকে ধরতে পারেনি তার অফিসে। অগত্যা গাড়িটা বার করে চলে এসেছিল যুদ্ধমন্ত্রকে। দুটো বাজার আর বাকিও ছিল না বিশেষ।
চওড়া সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসতেই দেখা হয়ে গেল কর্নেল ল্যান্সডেল-এর সঙ্গে। ধড়ে প্রাণ আসে প্যাশ-এর। বলে, আরে, এই তো আপনি এখানে! আপনার অফিসে ফোন করে
-জানি। রেডিও-টেলিফোনে ওরা আমাকে জানিয়ে দিয়েছিল।
–কিন্তু কী ব্যাপার? হঠাৎ আপনাকে আর আমাকে—
না! আরও কয়েকজন আসছেন। এবং আসছেন মিস্টার ‘এক্স’!
ফেডারেল ব্যুরো অফ ইন্টেলিজেন্সের সর্বময় অজ্ঞাত বড়কর্তার অভিধা হচ্ছে ‘চিফ’। জনান্তিকে অফিসারেরা বলত মিস্টার ‘এক্স’। সমীকরণের অজ্ঞাত রহস্য!
লিফট বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে প্যাশ ভাবছিল–আজ তাহলে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হয়ে যাবে। নামটা না জানা যাক, চাক্ষুষ দেখা যাবে তাকে। কিন্তু ব্যাপারটা কী?
পঞ্চমতলে যুদ্ধসচিবের দফতর। লিফটের খাঁচা থেকে বার হওয়া মাত্র ওদের কাছে এগিয়ে আসে একজন সিকিউরিটি অফিসার। হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে, কর্নেল প্যাশ এবং কর্নেল ল্যান্সডেল নিশ্চয়! আসুন আমার সঙ্গে। এই দিকে।
***
প্রকাণ্ড কনফারেন্স রুম। এ-ঘরে একাধিক যুগান্তকারী অধিবেশন হয়েছে এককালে। টেবিলটায় বিশ-পঁচিশজন অনায়াসে বসতে পারে। বর্তমানে বসেছেন আটজন। কর্নেল প্যাশ ও ল্যান্সডেল, এফ. বি. আই.-য়ের চিফ, যুদ্ধমন্ত্রকের চিফ-অফ-স্টাফ জেনারেল মার্শাল, যুদ্ধনীতি পরিষদের দুজন ধুরন্ধর রাজনীতিক–ভ্যানিভার বুশ এবং জেমস্ কনান্ট। এছাড়া ছিলেন অ্যাটম-বোমা প্রকল্পের সর্বময় সামরিক কর্তা জেনারেল লেসলি গ্রোভস্ এবং ওপেনহাইমার। যুদ্ধ চলাকালে এ প্রকল্পের ছদ্মনাম ছিল : ম্যানহাটান প্রজেক্ট। তার অসামরিক সর্বময় কর্তা ছিলেন মার্কিন বৈজ্ঞানিক ডক্টর রবার্ট ওপেনহাইমার–যুদ্ধান্তে যাঁর নাম হয়েছিল ‘অ্যাটম-বোমার জনক’। জেনারেল গ্রোভসস্ ছিলেন তার সামরিক কর্তা। অ্যাটম-বোমার সাফল্যে এই গ্রোভস্ আর ওপেনহাইমার রাতারাতি জাতীয় বীরে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছেন! সহস্রাধিক বৈজ্ঞানিকের ছ বছরের পরিশ্রমের বৃকোদরভাগ যেন ভাগ করে নিতে চান ওই দুজনে।
কাঁটায় কাঁটায় দুটোর সময় পিছনের দ্বার দিয়ে প্রবেশ করলেন সমরসচিব স্টিমসন। সকলেই উঠে দাঁড়ায়। আসন গ্রহণ করে স্টিমসন সরাসরি কাজের কথায় এলেন : জেন্টলমেন। বুঝতেই পারছেন অত্যন্ত জরুরি একটা প্রয়োজনে আপনাদের এখানে আসতে বলেছি। সমস্যাটা কী এবং কীভাবে তার সমাধান সম্ভব সে কথা আপনাদের এখনই বুঝিয়ে বলবেন এফ. বি. আই. চিফ। আমি শুধু ভূমিকা হিসাবে দু-একটি কথা বলতে চাই। প্রথমেই জানিয়ে রাখছি : আপনাদের সমস্ত সাবধানতা সত্ত্বেও ম্যানহাটান-প্রকল্পের মূল তত্ত্ব রাশিয়ান গুপ্তবাহিনী পাচার করে নিয়ে গিয়েছে! হ্যাঁ, এতক্ষণে মস্কোতে রাশান নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্টের দল হয়তো হাতে-কলমে অ্যাটম-বোমা বানাতে শুরু করেও দিয়েছে!
বৃদ্ধ সমরসচিব থামলেন। প্রয়োজন ছিল। সংবাদটা পরিপাক করতে সময় লাগবে সকলের! কর্নেল প্যাশ-এর মনে পর পর উদয় হল কতকগুলি ভৌগোলিক নাম-ট্রিনিটি : হিরোশিমা : নাগাসাকি–নিউইয়র্ক : শিকাগো : ওয়াশিংটন …
না, না, এসব কী ভাবছে সে পাগলের মতো! সম্বিত ফিরে পেল যুদ্ধসচিবের কণ্ঠস্বরে : হ্যাঁ, এ বিষয়ে আজ আর সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আজ সকালেই প্রেসিডেন্ট একটি গোপন পত্র পেয়েছেন কানাডা থেকে। চিঠিখানা আমি খুঁটিয়ে পড়েছি। আমাদের এফ. বি. আই. চিফও পড়েছেন। তা থেকে আমাদের দুজনেরই ধারণা হয়েছে বিশ্বাসঘাতক নিঃসন্দেহে একজন বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক! হয়তো নোবেল-লরিয়েট! আমি শুধু বলতে চাই–অপরাধের হিমালয়ান্তিক গুরুত্ব অনুসারে আমরা দয়া করে ছেড়ে কথা বলব না, বলতে পারি না; কিন্তু আপনারা দয়া করে দেখবেন বিশ্ববরেণ্য কোনো বৈজ্ঞানিককে যেন এ নিয়ে অহেতুক লাঞ্ছনা ভোগ করতে না হয়। প্রেসিডেন্টের মত–এবং আমিও তার সঙ্গে একমত–ওই বিশ্বাসঘাতক বৈজ্ঞানিক বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় অপরাধটা করেছে! আমি প্রেসিডেন্টকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি–যেমন করেই হোক, ওই বিশ্বাসঘাতককে আমরা খুঁজে বার করব। আপনাদের কর্মদক্ষতায় আমার অগাধ বিশ্বাস।
এফ.বি. আই.-চিফের দিকে ফিরে এবার বললেন, প্লিজ প্রসীড!
যন্ত্রচালিতের মতো শিরশ্চালন করলেন চিফ। তার এ্যাটাচি-কেস থেকে একটা মোটা খাম বার করে টেবিলের ওপর রাখলেন। বললেন : সংবাদটা আমরা জেনেছি কানাডার প্রধানমন্ত্রী ম্যাকেঞ্জি কিং-এর একটি ব্যক্তিগত পত্র থেকে। তারিখ গতকালের। চিঠিখানা প্রেসিডেন্ট পেয়েছেন আজ সকালে। চিঠির সঙ্গে আছে কানাডা গুপ্তচর বাহিনীর প্রধানের একটি প্রাথমিক রিপোর্ট এবং রাশিয়ান-এম্বাসির খানকয়েক গোপন চিঠির ফটোস্টাট কপি।
শেষোক্ত জিনিসটা হস্তগত হয়েছে এইভাবে : গত ছয়ই সেপ্টেম্বর, অর্থাৎ আজ থেকে মাত্র নয় দিন আগে, অটোয়ায় অবস্থিত রাশিয়ান এম্বাসির একজন কর্মী ঈগর গোজেঙ্কো কানাডা-পুলিসের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চায়। গোজেঙ্কোর বয়স ছাব্বিশ, কানাডায় রাশিয়ান দূতাবাসে সে তিন বছর ধরে কাজ করছে। একটি কানাডিয়ান মেয়েকে সে ভালবাসে এবং তাকে বিবাহ করতে চায়। রাশিয়ান এম্বাসি তাকে সে অনুমতি দেয়নি। গোজেঙ্কো গোপনে মেয়েটিকে বিবাহ করে, তার একটি সন্তানও হয়। খবরটা রাশিয়ান গুপ্তচরবাহিনী জানতে পারে। গোজেঙ্কো মনে করেছিল তার জীবন বিপন্ন। বস্তুত তার ফ্ল্যাটে পাঁচই রাত্রে গুপ্তঘাতক হানা দেয়। কোনক্রমে পালিয়ে এসে গোজেঙ্কো কানাডা-পুলিসের কাছে আশ্রয়ভিক্ষা করে। যেহেতু রাশিয়া আমাদের মিত্রপক্ষ তাই কানাডার পুলিস-প্রধান তাকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করেন। মরিয়া হয়ে গোজেঙ্কো সরাসরি ম্যাকেঞ্জি কিং-এর সঙ্গে দেখা করে এবং তার হাতে তুলে দেয় ওই গোপন নথি! এরপর বাধ্য হয়ে তাকে আশ্রয় দেওয়া হয়। ওই গোপন নথিপত্র থেকে জানা যাচ্ছে, রাশিয়ান গুপ্তচর বাহিনী দীর্ঘ তিন চার বছর ধরে এই ফমূলা সংগ্রহের চেষ্টা করেছে এবং অতি সম্প্রতি–গত মাসে–তাদের সে চেষ্টা সাফল্য লাভ করেছে।
রিপোর্ট পড়ে আমি এই কয়টি সিদ্ধান্তে এসেছি :
প্রথমত : অ্যাটম-বোমা তৈরির যাবতীয় তথ্য অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। আকারে সেটি ফুলস্ক্যাপ কাগজের আট পাতা। তাতে একাধিক স্কেচ আঁকা ছিল এবং গাণিতিক অথবা রাসায়নিক সূত্রে ঠাসা ছিল। সমস্ত নথিটাকে মাইক্রোফিলমে সংক্ষিপ্ত করা হয় এবং একটি সিগারেটের প্যাকেটে হস্তান্তরিত করা হয়। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা যায়, বিশ্বাসঘাতক একজন অতি উচ্চমানের পদার্থবিজ্ঞানী, তিনি সম্পূর্ণ বিষয়টা জেনেছেন, বুঝেছেন এবং সবচেয়ে বড় কথা–তার চুম্বকসার প্রণয়ন করেছেন। আমি এ নিয়ে ডক্টর ওপেনহাইমারের সঙ্গে কথা বলেছি। তার মতে সহস্রাধিক বৈজ্ঞানিকের ছ বছরের সাধনাকে আটখানি পৃষ্ঠায় যিনি সংক্ষেপিত করতে পারেন তিনি একটি দুর্লভ প্রতিভা!
দ্বিতীয়ত : জানা গিয়েছে, বিশ্বাসঘাতক একক প্রচেষ্টায় সবকিছু করেছে। ফলে সে শুধু পরমাণু বিজ্ঞান আর গণিতই নয়, ফটোগ্রাফি এবং মাইক্রোফিলম প্রস্তুতিপর্বও জানে!
তৃতীয়ত : বিশ্বাসঘাতক ইংরাজ অথবা আমেরিকান নয়। তার ছদ্মনাম ছিল ডেক্সটার।
চতুর্থত : মাইক্রোফিলমখানা 11.8.45 তারিখের সন্ধ্যায় হস্তান্তরিত হয়। তারিখটা নিশ্চয়ই মনে আছে আপনাদের। ওইদিন জাপান আত্মসমর্পণ করে। গুপ্তবার্তাটা যে লোক গ্রহণ করে সে হয় আমেরিকান, নয় ইংরেজ। তার ছদ্মনাম ছিল রেমন্ড।
এ-ছাড়া আর কোনো তথ্য এ পর্যন্ত জানা যায়নি। এনি কোয়েশ্চেন?
জেনারেল মার্শাল বললেন, ডেক্সটার যে মার্কিন বা ইংরেজ নয়, এ সিদ্ধান্তে কেমন করে এলেন?
চিফ বললেন, রাশিয়ান এম্বাসিকে ক্রেমলিন নির্দেশ দিচ্ছে, যেহেতু ডেক্সটারের মাতৃভাষা ইংরাজি নয়, তাই সে যেন প্রকাশ্যে রেমন্ডের সঙ্গে বাক্যালাপ না করে। তার উচ্চারণ শুনে লোকে বুঝতে পারবে সে বিদেশি। এ থেকে আমার অনুমান-ডেক্সটারের যেটা মাতৃভাষা, যে ভাষায় সে অনর্গল কথা বলতে পারে, সেটা জানা ছিল না রেমন্ডের।
–আই সী!
উপদেষ্টা-পরিষদের সদস্য জেমস্ কনান্ট এবার প্রশ্ন করেন, জেনারেল গ্রোভসস, আপনি বলতে পারেন ম্যানহাটান প্রজেক্টে যে-কজন বিদেশি বৈজ্ঞানিক কাজ করেছেন তাদের মধ্যে কতজনের পক্ষে এ-কাজ করা সম্ভবপর?
জেনারেল গ্রোভসস্ তৎক্ষণাৎ জবাব দেন, এ প্রশ্নের জবাব আমার চেয়ে ডক্টর ওপেনহাইমারই ভাল দিতে পারবেন–কারণ তিনি ওইসব বৈজ্ঞানিকদের আরও ঘনিষ্ঠভাবে চেনেন, তাছড়া কাজটা যে কতখানি শক্ত তাও তিনি আমার চেয়ে ভাল বুঝতে পারবেন।
ডক্টর ওপেনহাইমার একটু ইতস্তত করে বলেন, ম্যানহাটান-প্রকল্পে কয়েকশত ওই জাতের বিদেশি কাজ করেছেন; কিন্তু তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক পদার্থবিজ্ঞানীকে আমরা প্রতিটি বিভাগে ঢুকবার অনুমতি দিয়েছিলাম। ফলে তারা নিজ নিজ বিভাগের সংবাদই রাখতেন। সব বিভাগের সব কথা জানতে পারেননি। আপনারা জানেন, ম্যানহাটান প্রকল্পের অন্তত দশটি প্রধান শাখা তিন-চার হাজার মাইল দূরত্বে ছড়ানো ছিল। এমন একটি রিপোর্ট তৈরি করতে হলে ওই দশটি কেন্দ্রের অন্তত সাতটির খবর তাকে জানতে হয়েছে–সেই সাতটি কেন্দ্র হচ্ছে–কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বার্কলে, হানফোর্ড, শিকাগো, ওক রিজ, ডেট্রয়েট এবং লস এ্যালামস। এমন ব্যাপক জ্ঞান সংগ্রহ করতে পেরেছেন মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র, ধরুন দশ-পনেরো জন। তার বেশি কখনই নয়।
–আপনি কি দয়া করে সেই দশ-পনেরো জনের নাম আমাদের জানাবেন?
–জানাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তার পূর্বে আমি বলে রাখতে চাই কোনো সন্দেহের বশবর্তী হয়ে আমি কিন্তু কারও নাম বলছি না। এঁদের প্রত্যেককেই আমি বৈজ্ঞানিক হিসাবে শ্রদ্ধা করি এবং বিশ্বাসভাজন বলে মনে করি। এটা নিছক ‘অ্যাকাডেমিক ডিস্কাশান’–অর্থাৎ আমি উচ্চারণ করছি সেই কয়েকজন বিদেশি বৈজ্ঞানিকদের নাম, যাঁরা ইচ্ছা করলে এমন একটি গোপন নথি প্রস্তুত করবার ক্ষমতা রাখেন। অর্থাৎ কোন্ কোন্ বিদেশি বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান ওই উচ্চস্তরে পৌঁছাতে পারে–আর কিছু নয়।
–নিশ্চয়। আমরা বুঝেছি, এ কোন অ্যাসপার্শান নয়। বলুন?
-হাঙ্গেরিয়ান পদার্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে আছেন তিনজন–ফন নয়ম্যান, ৎজিলাৰ্ড এবং টেলার, রাশিয়ান দুজন–জর্জ ক্রিস্টিয়াকৌস্কি এবং রোবিনোভিচ, জার্মানির তিনজন- রিচার্ড ফাইনম্যান, হান্স বেথে, এবং জেমস্ ফ্রাঙ্ক। এছাড়া অস্ট্রিয়ান ভিক্টর ওয়াইস্কফ, ইটালির ফের্মি, ব্রিটিশ জেমস চ্যাডউইক এবং ডেনমার্কের নীলস বোহর। এই বারোজন!
বৃদ্ধ স্টিমসন দু-হাতে মাথা রেখে চোখ বুজে বসেছিলেন। তিনি যে ঘুমিয়ে পড়েননি তার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন হঠাৎ তিনি আপনমনে বলে ওঠেন, ও গড! হোয়াট এ ম্যাগনিফিসেন্ট লিস্ট টু ফাইন্ড আউট এ ট্রেইটার!
ডক্টর ওপেনহাইমার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলেন, বেগ য়োর পাৰ্ডন স্যার?
-বলছিলাম কি, ওই বারোজনের কত পার্সেন্ট নোবেল-লরিয়েট?
–প্রায় ফিফটি পার্সেন্ট স্যার! পাঁচজন!
–আপনি তো ওই সঙ্গে প্রফেসর আইনস্টাইনের নামটা করলেন না ডক্টর?
-না। তার কারণ, প্রফেসর আইনস্টাইন কোনদিন ম্যানহাটান-প্রজেক্টের কাঁটাতারের বেড়া পার হননি। না হলে ম্যানহাটান প্রকল্পের চুম্বকতত্ত্ব আটপাতার ভেতর সাজিয়ে দেবার ক্ষমতা আরও অনেকের কাছে। জার্মানির অন্তত পাঁচজন বৈজ্ঞানিক সে ক্ষমতার অধিকারী–প্রফেসর অটো হান, ম্যাক্স বর্ন, ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক, ওয়াইৎসেকার, অথবা হেইজেনবের্গ। হয়তো জাপানের প্রফেসার নিশিনাও পারেন।
–আই সী! বাই দ্য ওয়ে ডক্টর–এবার যে নামগুলি বললেন তার কত পার্সেন্ট নোক্ল-লরিয়েট?
–এইট্টি পারসেন্ট! এই পাঁচজন জার্মান বৈজ্ঞানিকদের ভিতর চারজনই নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন স্যার।
বৃদ্ধ নিঃশব্দে শুধু মাথা নাড়লেন। আবার চোখ দুটি বুজে গেল তার।
–এনি মোর কোয়েশ্চেন? প্রশ্ন করেন চিফ।
হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় কর্নেল প্যাশ। সর্বকনিষ্ঠ সে-বয়সে এবং পদমর্যাদায়। বলে, মাফ করবেন, কিন্তু রিপোর্টের ওই লাইনটা তো’রেড-হেরিং’ও হতে পারে?
-কোন লাইনটা? আর ‘রেড-হেরিং’ বলতে?
-ওই যে বলা হয়েছে ডেক্সটারের মাতৃভাষা ইংরাজি নয়, ওটা হয়তো ওরা ইচ্ছে করেই লিখেছে। ভেবেছে, যদি কখনও ওই দলিলটা আমাদের হাতে পড়ে তবে আমরা কোনোদিনই আর প্রকৃত অপরাধীকে খুঁজে পাবে না।
কেউ কোনো জবাব দেয় না। এমনটা আদৌ হতে পারে কিনা সবাই তা ভাবছে।
জেনারেল মার্শাল বলেন, এমন কথা হঠাৎ মনে হল কেন তোমার? তুমি কি ওই বারোজনের সঙ্গে কোনো ইংরেজ বা আমেরিকানের নাম যুক্ত করতে চাইছ?
– নো নো স্যার। নট এক্সাক্টলি দ্যাট!–সলজ্জে বলে কর্নেল প্যাশ।
বৃদ্ধ সমরসচিব আবার চোখ খুললেন। বললেন, ইয়ংম্যান, তোমার কথার মধ্যে কিন্তু একটা ইঙ্গিত ছিল! তাছাড়া এই বারোজনের লিস্টটাও কেমন যেন অসম্পূর্ণ মনে হচ্ছে আমার কাছে। বাইবেলের নির্দেশ তা নয়! তুমি আর কিছু বলবে?
দৃঢ়স্বরে মাথা নাড়ে প্যাশ : নো স্যার। আই…আই উইথড্র!
বিড়ম্বনার চূড়ান্ত।
***
ঘর থেকে বেরিয়ে নিচে নেমে এসে কর্নেল ল্যান্সডেল বলে, তুমি বেমক্কা অমন একটা কথা বলে বসলে কেন হে?
পুনরায় লাল হয়ে ওঠে প্যাশ। বলে, কী জানি! ও কথা বলা বোধহয় বোকামিই হয়েছে আমার।
-তা হয়েছে। এসব জায়গায় ভেবেচিন্তে কথা বলতে হয়।
ওরা ধীরপদে এগিয়ে আসে পার্কিং জোন-এর কাছে। প্যাশ গাড়িতে উঠতে যাবে হঠাৎ একটি অফিসার এসে বলে, এক্সকিউজ মি আপনাকে আবার উপরে ডাকছেন।
–কে ডাকছেন?–চমকে ওঠে কর্নেল প্যাশ।
–যুদ্ধসচিব।
ততক্ষণে কর্নেল ল্যান্সডেলও চলে গেছে। এ কী যন্ত্রণা! আবার কেন? বাধ্য হয়ে আবার ফিরে আসতে হল। সেই ঘরেই। ঘর এখন প্রায় শূন্য। বসে আছেন শুধু দুজন। যুদ্ধসচিব স্টিমসন এবং এফ. বি. আই. চিফ! সসম্ভ্রমে অভিবাদন করল কর্নেল প্যাশ।
–টেক ইয়োর সীট প্লিজ–বললেন বৃদ্ধ।
উপবেশন তো নয়, চেয়ারের গর্ভে আত্মসমর্পণ করল প্যাশ।
চিফ বললেন, এবারে বল। হঠাৎ ও কথা মনে হল কেন তোমার?
–আমি…মানে, আমার স্যার ও-কথা বলা বোধহয় ঠিক হয়নি!
–বি ক্যানডিড কর্নেল। ডক্টর ওপেনহাইমার যদি নীলস বোহর, হ্যান্স বেথের নাম বলতে পারেন, তবে তুমিই বা এত ইতস্তত করছ কেন? কোনো ইংরাজি-ভাষীর নাম কি মনে পড়েছিল তোমার?
হঠাৎ পূর্ণদৃষ্টিতে প্যাশ তাকিয়ে দেখল ওই অজ্ঞাতনামা লোকটির দিকে। ওর চিফ-এর দিকে। গম্ভীরভাবে বলল, ইয়েস স্যার।
–কী নাম তার?
–ডক্টর রবার্ট জে. ওপেনহাইমার!
চিফ একবার অপাঙ্গে তাকিয়ে দেখলেন যুদ্ধসচিবের দিকে। বৃদ্ধ নির্বিকার।
-তুমি এবার যেতে পার–বললেন চিফ। ক
র্নেল প্যাশ পুনরায় অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে আসে।
বৃদ্ধ যুদ্ধসচিব এতক্ষণে চিফের দিকে ফিরে বললেন : থ্যাঙ্ক গড! দ্যাট ম্যাড গাই ডিডন্ট মেনশন মাই নেম, অর দ্যাট অফ হ্যারি ট্রুম্যান!
***
পরদিন সকালে জেনারেল গ্রোভসস্ নিজেই এলেন যুদ্ধসচিবের দফতরে। একখানি ফাইল বৃদ্ধের সামনে মেলে ধরে বললেন, পয়েন্টস্ অফ রেফারেন্সগুলি একটু দেখে দিন।
–কিসের পয়েন্টস?
–এ্যাটমিক-এনার্জি এম্পায়োনেজ ব্যাপারে আমরা এফ. বি. আই.কে কোন্ কোন্ বিষয়ে তদন্ত করে দেখতে বলব।
পড়ে যান, শুনি।
–প্রথমত-ম্যানহাটান এঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্ট থেকে আদৌ কোনো গোপন তথ্য বেরিয়ে গেছে কিনা। গিয়ে থাকলে, কতদূর খবর পাচার হয়েছে? দ্বিতীয়ত কে বা কে-কে এই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে? তৃতীয়ত-কানাডার প্রধানমন্ত্রীর পত্রের যাথার্থ্য। চতুর্থত, বিশ্বাসঘাতক কী পরিমাণ উৎকোচ গ্রহণ করেছে? এবং, পঞ্চমত, কোন্ বিদেশি সরকার এই গুপ্তচরবৃত্তিতে উৎসাহ জুগিয়েছে?
–আমার তো মনে হয় ঠিকই আছে।
কাগজখানিতে অনুমোদনসূচক সই করে ফেরত দিলেন যুদ্ধসচিব। তারপর বললেন, বাই দ্য ওয়ে জেনারেল, কাল ওই ম্যাড গাই যে কথাটা বলেছিল সে বিষয়ে আপনার কী ধারণা? কোনো ইংরাজ বা আমেরিকান কি ডেক্সটারের ভূমিকায় নামতে পারে?
–অসম্ভব নয় স্যার। হয়তো সত্যিই ওই লাইনটা একটা ‘রেড-হেরিং। ডেক্সটারের মাতৃভাষা ইংরাজিই–আমাদের বিপথে চালিত করার জন্য ওই পংক্তিটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে লেখা হয়েছে।
তার মানে দাঁড়াচ্ছে–কাল আমরা যে বারোজনের তালিকা নিয়ে আলোচনা করছিলাম আসল অপরাধী তার ভিতর নাও থাকতে পারে?
–ওই অনুমান সত্য হলে তাও সম্ভব স্যার।
-একটা কথা। ম্যানহাটান-প্রজেক্টে যেসব প্রথম শ্রেণির অসামরিক বৈজ্ঞানিকদের নিযুক্ত করা হয়েছিল, তাদের নিয়োগের পূর্বে প্রতিটি ক্ষেত্রেই তো এফ. বি. আই.-কে দিয়ে সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স করানো হয়েছে?
–নিশ্চয়!
–ওই বারোজনের মধ্যে এমন কেউ কি আছেন যাঁর ক্লিয়ারেন্স দিতে এফ. বি. আই. আপত্তি জানায়?
–না। আমি কাল রাত্রেই অফিসে ফিরে ওই বারোজনের ব্যক্তিগত ফাইল খুঁটিয়ে দেখেছি। প্রত্যেকেরই সিকিউরিটি-ক্লিয়ারেন্স আছে।
-ধন্যবাদ!
জেনারেল গ্রোভসস্ কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে আসছিলেন। হঠাৎ কী মনে করে থেমে পড়েন। বলেন, একটা কথা স্যার। কথাটা স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই এ-সময়ে বলে রাখতে চাই, যদিও আপনি এ প্রশ্ন করেননি
-ইয়েস জেনারেল?
–ওই বারোজনের ক্লিয়ারেন্স সম্বন্ধে আপত্তিকর কিছু না থাকলেও তার বাইরে একজন টপ-র্যাঙ্কিং বৈজ্ঞানিক আছেন, যিনি প্রতিটি প্রজেক্টের ভিতরে গিয়েছেন এবং গোপনতম সংবাদ জেনেছেন–যাঁর ক্লিয়ারেন্স এফ. বি. আই. দেয়নি
-ইস ইট? কার কথা বলছেন আপনি?
–ডক্টর আর. জে. ওপেনহাইমার!
বৃদ্ধের ভ্রূযুগলে ফুটে উঠল কুঞ্চন। কাঁচের কাগজচাপাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, স্ট্রেঞ্জ! এফ. বি. আই.-য়ের ক্লিয়ারেন্স ছাড়া কেমন করে তাকে ওই সর্বোচ্চ পদে বসানো হল?
-এফ. বি. আই. য়ের ক্লিয়ারেন্স ছাড়াই তাকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছিল। যিনি দেন, তিনি ওই বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। প্লেনিপোটেনশিয়াল মিলিটারি অথরিটি।
–আই সী! তিনি কে, জানতে পারি?
–আমি নিজেই স্যার!
–হু!
বৃদ্ধ আবার চুপ করে যান। জেনারেল গ্রোভসস নীরবে অপেক্ষা করেন। বৃদ্ধ পুনরায় বলেন, সেক্ষেত্রে দয়া করে একবার ডক্টর ওপেনহাইমারের পার্সোনাল ফাইলটা আমাকে পাঠিয়ে দেবেন?
নিশ্চয়ই দেব, স্যার!
বিদায় নিয়ে চলে আসছিলেন জেনারেল গ্রোভসস, হঠাৎ পিছন থেকে তাকে আবার ডাকলেন যুদ্ধসচিব : আই সে জেনারেল, অমার মনে হয় পয়েন্টস্ অফ রেফারেন্সের ওই চার-নম্বর আইটেমটা নিষ্প্রয়োজন। ওটা আমাদের জানা আছে।
চমকে ওঠেন গ্রোভস। বলেন, বিশ্বাসঘাতক কী পরিমাণ অর্থ উৎকোচ হিসাবে, পেয়েছিল তা আপনার জানা আছে স্যার?
–আই থিংক সো। একটু অঙ্ক কষতে হবে। ত্রিশ ‘ডুকাট’ উনিশ শ’ বছর ফিক্সড ডিপোজিটে রাখলে সুদে-আসলে কত রুবত্স হয় সেটা হিসাব করে বার। করা শক্ত নয়! বারোজন নয়, এখন তো আমরা তেরোজনের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করছি!
জেনারেল গ্রোভসসও খ্রিস্টান, কিন্তু তিনি নিতান্তই সামরিক অফিসার। এ উক্তির তাৎপর্য ধরতে পারেন না। বৃদ্ধ কিন্তু ততক্ষণে কাগজপত্রের মধ্যে ডুবে গিয়েছেন।