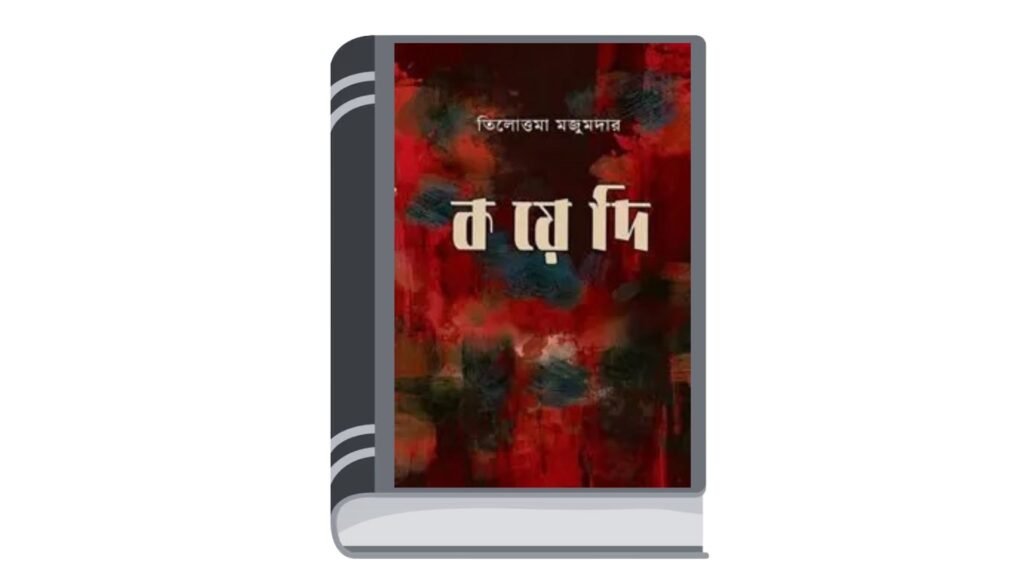কয়েদি – ৩
৩
সম্রাট আলেকজান্ডার, আমার চোখে তুমিই মহান, তুমি উদার, ক্ষমতার মোহে অন্ধ নও, ক্ষমা ও ধৈর্য তোমার শক্তি। বলো সম্রাট, তুমি কি একমত?
একেকবার একেক প্রশ্ন তাকে শুয়ে পড়তে বাধ্য করে। শোয়া-বসা ও ফুট আষ্টেক জায়গায় হাঁটা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। হাঁটতে সে স্বচ্ছন্দ নয়। পায়ে ভারী শেকল ও বেরি। বাঁধা থাকলে নিজের ছন্দ অনুযায়ী কেউ চলতে পারে না। বসাও কষ্টদায়ক। শুয়ে থাকলে, সে যখন পার্শ্ব ফেরে, শেকলও পার্শ্ব পরিবর্তন করে দ্বিতীয় সত্তার মতো।
এত বছরেও শেকলকে নিজের অংশ করে নিতে সে সক্ষম নয়। চেষ্টাও করেনি। এই আধুনিক বিশ্বে, যখন মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে সরব মানুষ, এবং সেইসঙ্গে ইচ্ছামৃত্যুর পক্ষেও ধ্বজা তোলা হচ্ছে, তখন আদিম শেকল উচ্ছিন্ন করার আন্দোলন কি হতে পারে না আরও এক মুক্তির পথ?
ধরা যাক শেকল ভেঙে বৈপ্লবিক জয়ান্তে কেউ রাজা হল, বা শাসক, রাষ্ট্রীয় প্রধান, আর সেই শাসনের বিরুদ্ধে আবার প্রতিরোধ ও আন্দোলন ঘনিয়ে এল, তখন সেই শেকল-ভাঙা রাজা পুনরায় শেকলের কাছে পৌঁছে যাবে। দ্রোহীর জন্য তুলে নেবে তারই ফেলে যাওয়া শেকল। তাহলে শেকলকে শাসন ও প্রতিবাদ দ্বৈরথের কেন্দ্র বলা যায়। অথবা পিপে হয়ে উঠতে পারে বৈরাগ্য এবং ত্যাগের আশ্রয়। আমার ঘর নেই সংসার নেই জড়িয়ে রাখবার কিছু নেই ছেড়ে দেবারও কিছু নেই, তাহলে তোমার আদেশ তুমি কোথায় আরোপ করবে?
সেদিক থেকে দেখতে গেলে হতদরিদ্ররাই মুক্ত মানুষ। সম্পদকুলীন সমাজ তাদের ডুবন্ত দশায় আঁকড়ে ধরার জন্যও কুটোটি দিতে নারাজ, তাই ছাড়ারও কিছু নেই। তবে ধরা-ছাড়ার মধ্যে একটি বস্তু থাকে। পিঠের চামড়া, মেরুদণ্ড আর পাকস্থলী সমেত বেঁচে থাকা একপ্রকার জ্যান্ত মানুষের জীবন। রাজা স্বয়ং ন্যাংটো হলেও তাঁকে ওই জ্যান্ত মানুষের জীবন থেকে পাকাপাকি বাদ দেওয়া যায় না, কারণ রাজার পোশাক থাকলে তিনি দার্শনিকের বাণী শোনার জন্য স্বয়ং আসেন পিপে অবধি, সিংহাসন থেকে নেমে। আর দার্শনিক নির্ভয়ে বলেন, রাজা, সরে দাঁড়াও। সূর্যের আলো আড়াল করেছ তুমি। আমার কাছে আলো আসতে দাও।
আলো আসতে দাও রাজা। আলো আসতে দাও হে অধিপতি। আসতে দাও আলো ওগো মহীপতি। সমস্ত মোহত্যাগী আমি মুক্তির আলো নিয়ে বেঁচে আছি দেখো।
সম্মান ও ক্ষমা দিয়ে অবজ্ঞা করেছিলেন আলেকজান্ডার ওই দার্শনিককে।
তখন, রাজা, পোশাকে নিজেকে ঢেকে রাখার সাফল্যে আত্মবিশ্বাসী। তিনি জানেন, দারিদ্র্যের আরাধনাও প্রকৃতির ধর্মের বিরুদ্ধাচার। তিনি জানেন চূড়ান্ত মুক্তি বলে কিছু হয় না। সেই সত্য আড়াল করে তিনি তুলে নেন ঝকঝকে সাহসী কুঠার।
ন্যাংটো, নোংরা, লোকের গায়ে প্রস্রাব করে দেওয়া ডায়োজেনেস, নিজের উলঙ্গপনা যাপন করে খুলে দিয়ে গেলেন রাজার উলঙ্গ হওয়া নৈতিকতা ও দারিদ্র্য জারি রাখার অধিকার। আর যে রাজা উলঙ্গ, তাঁর প্রয়োজন কাকপক্ষী চুপ করিয়ে রাখার জন্য সন্ত্রসন। তাই তাঁর হাতে থেকে যায় শোষণ, পীড়ন, অত্যাচারের আদেশ ও মৃত্যুদণ্ডের ক্ষমতা।
সেই ক্ষমতা মিথ্যা ও ভঙ্গুর।
সেই ক্ষমতা উলঙ্গপনার দুর্বল হীনতার আশ্রয়ে নিপীড়নে ঢেকে রাখতে চায় ক্ষমতা হারানোর ভয়। উলঙ্গ শাসকের দল মুক্তি ও সত্য ছুঁতে ভয় পায়। কখনো মোড়ক খুলে দেখে না ওই বস্তু আসলে কী। কিংবা কত কিছু না-হওয়া। কতখানি পূর্ণ, কতখানি শূন্য।
যে যতই মুক্ত হোক, যে যতই হোক সত্যবান, রাজা ক্ষমতাবলে পিঠের চামড়া তুলে ফেলতে পারেন। ভেঙে দিতে পারেন মেরুদণ্ড। অ্যাসিডে পুড়িয়ে দিতে পারেন পাকস্থলী, যাতে ক্ষুধা বলে কিছু না থাকে।
তাহলে দাঁড়াচ্ছে কী?
পুবের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠল, ‘পিপেয় ঢুকে মুক্তপুরুষ হয়ে থাকলেই চুকে যায় না। মুক্তি বজায় রাখার জন্য ক্ষমতা অর্জন করতে হয়। যেকোনও রাষ্ট্র তাই ক্ষমতা বাড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করে। সামরিক, অর্থনৈতিক, দর্শন ও সাংস্কৃতিক। এবং দেখো, রাজা সাহসী হোন আর ভিতু, রাজা বহুমূল্য পোশাক পরুন আর ন্যাংটো থাকুন, সত্য ও মুক্তি বিষয়ে তাঁদের ধারণায় তা প্রভাব বিস্তার করে না। সত্য জেনে কেউ ভীত হয়, কেউ নির্ভীক। মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় কেউ ত্রস্ত, কেউ বেপরোয়া।’
বইগুলি তার দিকে অভিমানী চোখে তাকিয়ে থাকল। আঁকাবাঁকা ছবির প্রচ্ছদ। এলোমেলো অক্ষরমালা। ওই দেওয়ালের প্রতি তার আর আগ্রহ নেই। বহু দর্শনের বই পড়ে সে এই কুঠুরিতে স্থিত শেকলে বাঁধা। তার জন্য পুবের দেওয়াল কিছুমাত্র দায়ী নয়। সে ওই দেওয়ালকে বলে জ্ঞান। যা নৈর্ব্যক্তিক, স্বয়ংসিদ্ধ, নাভিকুণ্ডের মতো অদাহ্য। জ্ঞানের প্রতি টুকরো মন্তব্য করে সে নিমগ্ন থাকে উত্তরের দেওয়ালে। তার উত্তরায়।
এখন তার ইচ্ছে হল, এই কথাটি সে দক্ষিণের দেওয়ালকে বলে। তার মুখ বেঁধে রাখা নেই। জিভ কেটে ফেলেনি। গলাও টিপে ধরেনি কণ্ঠরোধ উদ্দেশে। ইচ্ছে হলেই সে কথা বলতে পারে। বলল।
‘আমি দেওয়াল বাওয়া শিখতে পারলাম না। কতবার চেষ্টা করেছি। মেঝে থেকে কমোডের ঘাড়ে। তারপর সিস্টার্নে। আবার কমোডে। মেঝেতে।’ ঘড়ঘড়ে স্বরে সে বলল।
দক্ষিণের দেওয়াল, যার নাম দিয়েছে সে বন্ধু, বা নাম দেওয়া নয়, ওই দেওয়ালের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে যাবার পর, যেহেতু বন্ধুকে নাম ধরে না ডেকেও চলে যায় আজীবন, সেহেতু, বন্ধুই হয়ে গেল সম্পর্কের নাম ও সংজ্ঞা, সেই বন্ধু বলল, ‘এই তো, কতদিন পর কথা বললে। আজকাল চুপ করেই থাকো।’
‘মনে হয়, কথা ভুলে যাচ্ছি। কাল রাতে কী হল শোনো। হঠাৎ পা সোজা করতে পারি না, হাঁটুর ভাঁজে যেন নিজের শিরা নিজেকেই রজ্জুবন্ধন দিয়েছে। যন্ত্রণা। ভীষণ যন্ত্রণা। পা-কে নির্দেশ দিচ্ছি, সোজা করো, ওটা সোজা করো। কী সোজা করব? কী? পায়ের সে কী মেজাজ। বললাম, ওটা, ওটা, ওই যে ওই, কী মুনি যেন? জহ্নু। ধ্যাত্তেরি। বলো-না। আরে যে আস্ত গঙ্গা মুখ দিয়ে পান করে কান দিয়ে বার করেছিল। উফফ। জানু। জানু? তখন গিয়ে পায়ের টনক নড়ল। ওঃ, হাঁটু? তা-ই বলো। তারপর সেই নিয়ে দুই পায়ের কী হাসাহাসি। এ ওর বেড়ি ধরে টানে তো ও এর শেকল নেড়ে দেয় যেন চিবুকে চুমু খাচ্ছে।’
‘ব্যথা কমল? কোন পায়ে?’
‘কোন পায়ে যেন? ভুলে গেছি। কী এসে যায়? ডান-বাম দুই সমান।’
‘তা-ই আবার হয় নাকি? দক্ষিণের দেওয়াল যা, উত্তরের দেওয়ালও কি তা-ই?’
‘মাঝে মাঝে সব একাকার হয়ে যায়, বুঝলে কিনা। বন্ধু আর শত্রু আলাদা করতে পারি না। অবশ্য এখন আর আমার শত্রু নেই কোথাও। যতটুকু যা আছে, সব বন্ধু। আমি তো বাইরে নেই কতকাল। শত্রুদের মুশকিল হল, প্রতিপক্ষকে উত্ত্যক্ত করতে না পারলে, ভয় দেখাতে না পারলে, ক্ষতিসাধনে নিরন্তর প্রবৃত্ত না হতে পারলে তাদের বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য হারিয়ে যায়।’
‘আমার তো মনে হয়, তোমার শরীর তোমার শত্রু হয়ে উঠছে। নইলে নিজের হাঁটুর যন্ত্রণায় নিজের পা কখনো হাসাহাসি করে? আর তোমার স্মৃতিশক্তি? সে-ই বা কীরকম লোক? হাঁটু মনে করতে গিয়ে গঙ্গা যমুনা শিব কপিল মুনি কত কী ভাবিয়ে তুলল। একজন যন্ত্রণাকাতর মানুষকে এরকম করতে হয়?’
‘তোমার কি মনে হয় বলো তো? এসবই চক্রান্ত? মস্ত চক্রান্ত? যাতে মুক্তি পেয়ে ওর কাছে যেতে না পারি? বুঝলে, ওই যে আমার পদযুগল, ওরা জেলখানার শেকলে বাঁধা থাকতে থাকতে ওদের লোক হয়ে গেছে। ওরা যে বন্দি, সেই কথা ভুলে ক্ষমতাসীনের সঙ্গ পেয়ে পেয়ে ভাবতে শুরু করেছে ওরাও শেকল। হাহ, যখন ওই শেকল খুলে যাবে, মুক্ত হয়ে যাব আমি, কী হবে তখন? আমি ওদের চলতে বাধ্য করব না? নিয়ে যাব না সেই সেইখানে? ওর কাছে? চলতে না চাইলে বেদম পিটব।’
‘ও হে বন্ধু, তুমি কি বলতে চাও, আমিও তোমায় পাহারা দিতে দিতে ওদের লোক হয়ে গেছি?’
‘কথাটা গায়ে যখন মাখলে তখন সত্যই বলতে হবে। অবশ্য কতকাল হল আমি মিথ্যে বলতেও ভুলে গেছি। প্রয়োজন হয় না।’
‘সত্যিটা কী, শুনি?’
‘সত্যিটা হল, তুমি ওদের লোক, আসলেই ওদের লোক। কিন্তু আমার প্রহরা দিতে দিতে হয়ে গেছ সহৃদয় দেওয়ালবান্ধব। আমার প্রিয় বন্ধু। সে বিষয় নিয়ে এমন গোলমাল হওয়া তোমার পক্ষে ক্ষতিকারক। কোথাও বেফাঁস বলে ফেললে তোমার বেতন হয়তো কাটা যাবে না কিন্তু অবসর ভাতা দেওয়ার সময় অসভ্যতা সৃষ্টি হতে পারে। পা থেকে শেকল খুলে গেলে পা যেমন পুনরায় আমার ইচ্ছেদাস, অন্যান্য অঙ্গের মতোই, তেমনই, তুমি যখন পদ হতে অবসর নাও, তখন তুমিও পদাধিকারীগণের ইচ্ছেদাস।’
‘নিজের পায়ের ওপর রাগ রেখো না বন্ধু। পা হল গতির গতি। তোমার সঙ্গে বন্দি থেকে তার খানিক বিরস লাগলে বলার কিছু থাকে না। জেলখানায় পাহারাদার মস্তি করে খইনি চাপড়ালে কয়েদি কাতর চক্ষে দেখে আর বলে, টুকচা পাব না দাদা? প্রসাদ? হয় হয়। খইনি, ভাব, ভালোবাসা, মতামত বিনিময় হয়। তেমনই তোমার পা ও শেকল বেড়ি। একঘেয়েমি কাটাতে খানিক হাসাহাসি করে। বন্ধুরাও তো করে এমন। আমিও কি করি না?’
‘না না। তুমি আমায় নিয়ে কখনো হাসাহাসি করো না। বন্দি মানুষের গায়ে চাবুকের মারের চেয়ে বেশি এসে লাগে ব্যঙ্গ, এই কথা তুমি সবসময় মনে রেখেছ।’
‘আর উত্তরা? তাঁর কথা কী বলবে?’
‘উত্তরা, উত্তরা আলাদা। ও কারো মতো নয়। তুমি তো জানো। মুক্তি পেলে আমি উত্তরার কাছে চলে যাব।’
‘তুমি নিশ্চিত, তিনি আজও তোমার অপেক্ষায় আছেন?’
‘সন্দেহের কোনও কারণই নেই। তোমাকে বলেছি না? ও আমাকে ভালোবাসে? ও অপেক্ষা করে আছে আমি এই কয়েদখানা থেকে বেরুলেই ও আমাকে নিজের কাছে নিয়ে যাবে।’
‘এই লোহার শেকল খুলতে পারবে কি?’
‘শেকল একদিন আপনি খুলে যাবে।’
‘শেকল খোলা মানেই মুক্তি?’
‘না বন্ধু। মুক্তি আর বন্ধন যেকোনও মুহূর্তে স্থানবিনিময় করতে পারে।’
‘তা পারে।’
‘আবার কখনো কখনো যাকে বন্ধন বলে মনে হয়, তা হঠাৎ ধরে মুক্তির রূপ। কিংবা উলটোটা।’
‘মুক্তি বলে যাকে মানো, সে-ই আসলে বন্ধন?’
‘ডায়োজেনেসের কথাই ধরো। নিন্দাবাদের মধ্যে তিনি মুক্তির পথ সন্ধান করছেন। কিন্তু সমাজের রীতি ও মানসিকতার প্রতি অবজ্ঞা, সন্দেহ, ঘৃণা, অবহেলা আত্মিক বিকাশের পথ হতে পারে না। তিনি সম্ভবত আত্মঘৃণার শিকার। নিজেকেই ঘৃণা করেন বলে তিনি দিনের আলোয় জ্বলন্ত বাতি হাতে হেঁটে যান। কী ব্যাপার ডায়োজেনেস? দিনের বেলায় বাতি হাতে চলেছ যে? একজন মানুষ খুঁজছি। ভাবো, কী অপমান। লোকটা কাউকে মানুষ বলে গণ্য করে না। সূর্যের কিরণও কোনও মানুষ খুঁজে পায়নি। এই লোকের বাতি কী করবে? অর্থাৎ আশপাশে কেউ মানুষ নয়। কেন? বলো, কেন? আমাদের চারপাশে সারাক্ষণ কত ডায়োজেনেস। নিন্দাবাদের মধ্যে তাদের বেঁচে থাকার সার্থকতা। ঘৃণার মধ্যে তাদের তৃপ্তি। তারা কি বন্দি নয়?’
‘যেহেতু তুমি প্রেম এবং বিশ্বাস, ক্ষমা এবং আস্থায় মুক্তি আছে মনে করো, তোমার দৃষ্টিতে নিন্দাবাদ শৃঙ্খল বটে।’
‘ডায়োজেনেস এক অসার্থক, উন্মাদ, বিকৃত মানুষ।’
‘কী এসে যায়?’
‘অবশ্যই যায়। লোকটা এক দর্শনের প্রণেতা। লোকটা একরাশ হাড়ের দিকে তাকিয়ে সম্রাট আলেকজান্ডারকে বলেছিল, ওই স্তূপে তোমার বাপের অস্থি আছে নাকি? আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না।’
‘ওঃ।’
‘ঠিক। ওই ওঃ বলা ছাড়া তুমি, আমার বন্ধু, তুমি সুসভ্য কারাপ্রাকার, কী আর করতে পারো? এখানে ডায়োজেনেস সম্রাটত্ব অবমানিত করে মুক্তির স্বাদ নিচ্ছে। মৃত্যুর পর সবাই মাটি হয়ে যাবে, মিশে যাবে পঞ্চভূতে, এই পরিণতি অনিবার্য বলে মৃত্যুর পূর্বেও সমস্ত অস্থি একাকার, এই সমীভবনের চিন্তা গভীর হীনমন্যতা, আত্মঘৃণার প্রকাশ। আমার আত্মকরুণা বা আত্মঘৃণা সহ্য হয় না। প্রেম, শ্রদ্ধা, ক্ষমা ও বিশ্বাস যার নেই, তাদের আমি উন্মাদ, বিকৃতমানস, হিংসুক ও স্বার্থান্বেষী বলে মনে করি। এরা কেউ মুক্ত নয়। কেউ স্বাধীন নয়। আমার শেকল খুলতে পারলেই আমি উত্তরার কাছে চলে যাব। শেকল খুলবেই, খুলবেই।’
‘আমাকে ফেলে যাবে?’
‘না। ফেলে যাব কেন? তুমি থাকবে আমার হৃদয়ে। বন্ধুকে কখনো ফেলে যাওয়া যায় না। তুমি যেখানেই যাও, সে তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। কিন্তু তোমার একটা অংশ, সে আমার বন্ধু নয়। সে সাজাপ্রাপ্ত কয়েদির রাষ্ট্রপ্রেরিত প্রহরী। আমি তাকে রেখে যাবার বা ফেলে যাবার কেউ নই। মেয়াদ ফুরোলে তোমার জায়গায় অন্য কেউ, আমার জায়গায় আর-একজন। দক্ষিণের দেওয়াল প্রহরী ভাবলেশহীন মুখ করে দাঁড়াবে, আর সেই নতুন বন্দি ভাববে কবে আমার মুক্তি হবে?’
‘নতুন কোনও অপরাধী কারাগারে অন্তরিন হলেই প্রহরী, কক্ষপ্রাকার, কঠিন ধাতব দরজায় জিনিসপত্র লেনদেন করার এই একফালি জানালা ও অন্ধকারে স্থিত কয়েদির মধ্যে একরকম নতুন সম্পর্ক তৈরি হতে থাকে। হয়তো বন্দি অনুশোচনা দিয়েই তার শাস্তির প্রথম ধাপ শুরু করল।’
‘তা হতেও পারে। তবে অনুশোচনা আসবেই এমন কোনও কথা নেই। কারো কৃতকর্ম সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা হতে পারে। কারো সময় লাগে। অনেক অনেক দিন। কারো অনুশোচনা বলে কিছু নেই আদৌ। সেরকম মানুষই কিন্তু বেশি। জেলের বাইরেও। তুমি কি মনে করো না, ডায়োজেনেসের প্রতিরূপ কোটি কোটি অপমানব প্রতিমুহূর্তে কত অনুশোচনাহীন অপরাধ করে যাচ্ছে?’
‘জানি।’
‘অপরাধ করেও যাদের অনুশোচনা আসে না, তারা কি জঘন্য রুদ্ধাত্মা নয়? তারা কি নয় জিয়ন্ত প্রাণশোষী প্রেত? তোমার আমার মুক্তির পথও তারা অবরোধ করে না কি?’
‘নিশ্চয়। কিন্তু মুক্তি তোমার কাম্য। আমার নিজেকে মুক্তই মনে হয়।’
‘ওঃ। তুমি মুক্ত। তা-ই না? কতশত অপরাধীর কক্ষপ্রাকার হয়ে দায়িত্ব পালন করছ তুমি মুক্তহৃদয়। তোমার কি কোথাও কখনো গমনের ইচ্ছা হয়?’
‘আমি ইচ্ছা ভুলে গেছি।’
‘সেই তো বন্দিদশা বন্ধু আমার।’
‘সেই মুক্তি বন্ধু। ইচ্ছাই তোমার সবচেয়ে কঠিন শেকল।’
‘না না না। ইচ্ছাই আমার মুক্তি। রইল বিরোধ তোমার সঙ্গে।’ ‘কিন্তু বাইরের অগণিত অননুশোচক শয়তানের তৈরি কঠোর বন্ধন তোমাকে পীড়িত করে না বলতে চাও?’
‘করে। নিশ্চয় করে।’
‘কৃত অপরাধের অনুশোচনা অপরাধীর হৃদয় শুদ্ধ করবে, এই ভাবনায়, জেলখানাকে বলা হচ্ছে সংশোধনালয়।’
‘তবে?’
‘এই প্রসঙ্গ সমস্তই পরস্পর সম্বন্ধন, আবার পৃথক। যেমন, তোমার চোখে যা মনোবিকার, ডায়োজেনেস তাকে বলেন মুক্তি। তুমি ইচ্ছাকে বলো মুক্তি, আমি বলি আমি মুক্ত ও স্বাধীন, কারণ আমার কোনও ইচ্ছা নেই। অর্থাৎ, মুক্তিও শর্তাধীন ও ব্যক্তিসাপেক্ষ।’
‘হায়, এ আমি কী করলাম! তোমাকে ডায়োজেনেসের নিন্দাবাদে দীক্ষা দিলাম আমি? ডায়োজেনেসের প্রতি আদ্যন্ত ঘৃণা সত্ত্বেও?’
‘দীক্ষিত যদি হয়ে থাকি, তোমার দ্বারা, সে তোমার সখ্যে বন্ধু। তোমার ভালোবাসার শক্তিতে।’
‘না না, দক্ষিণ, প্রিয় বান্ধব আমার, দয়া করে নিন্দাবাদ প্রশ্রয় দিয়ো না, দিয়ো না। মিস্যান্থোপি এক জঘন্য জিনিস। দেখো দেখো আমার শেকল, আমার পায়ের অস্থি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে চায়। তোমার মনে পড়ে, শেষ কবে আমার শয্যার উপকরণ বদলে দিয়েছিল? ওই আমার উপাধান। নরম বালিশে তুলোর বীজ থেকে বেরিয়ে এসেছে শক্ত খোলের পতঙ্গ। বালিশের গায়ে শ্যাওলা আর পোকাদের রাশি রাশি ডিম। আর, আর দেখো আমার বিছানার চাদর, তোশক, পচা মাংসের গন্ধ ভরে আছে। রাস্তার ভিখিরিও এর চেয়ে ভালো চাদরে শোয়। আমার ধারণা, ডায়োজেনেসের মদের পিপে এখানকার চেয়ে অনেক বেশি বাসযোগ্য ছিল। তবুও, তবুও আমি মানবীয় মাধুর্য বাঁচিয়ে রাখতে চাই। নিন্দা ও সন্দেহ মানুষকে জঘন্য কারাগারে বন্দি করে। সেই কারাগার চিন্তনে, সেই বন্দিশালা তাদের হৃদয়। ডিকেন্স, স্বয়ং ডিকেন্স বলছেন, নিন্দাবাদ আনন্দের ঘাতক।’
‘বন্ধু, তুমি যা নিয়ে জীবন যাপন করো, আমিও তা-ই নিয়েই করি। তোমার সমস্ত কথা আমি জানি। যা জানি না, বোলো তুমি। তোমার বিছানায় প্রতিটি কীট ও শৈবালের জন্ম-মৃত্যুর তথ্য রাখা আমার কাজ। তুমি সেখানে শয়ন করো, আমি দেখি। আমার মধ্যে নিন্দাবাদ প্রবেশের জায়গা নেই।’
‘কিন্তু চারিদিকে থিকথিক করছে বিবেকহীন অমানুষের দল, তারা তোমাকে প্রভাবিত করতে পারে। নিন্দা ও সন্দেহের পথ সহজ, আনন্দ ও বিশ্বাসের পথ কঠিন। বিবেকবর্জন আত্মসুখের সহায়, আত্মানুসন্ধান ও অনুশোচনা আত্মমোহের পরিপন্থী।’
‘যাদের অনুশোচনা নেই, তারা অন্য জাত। যাদের আত্মানুসন্ধানের সময় লাগে, তারা কি নিজের ভিতর প্রতিরোধক্ষমতা তৈরি করে নেয়? আত্মপক্ষ সমর্থনের?’
‘অপরাধের সঙ্গে আত্মপক্ষ সমর্থনের একেবারে সরলরৈখিক সম্পর্ক। তুমি পথেঘাটে এখানে-ওখানে দেখবে, ছোটোখাটো অপরাধ, যেগুলির জন্য কেউ নালিশ করতে থানায় ছোটে না, সেখানেও স্বপক্ষ সমর্থন থাকে। তাৎক্ষণিক স্বতোৎসারিত অনুশোচনা ও ক্ষমা প্রার্থনার শিক্ষা সভ্যতার প্রগতিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ অথচ বিরল বলেই আমার ধারণা। খুব কম লোক তা আয়ত্ত করতে শিখেছে। আমি দুঃখিত, আমার অন্যায় হয়েছে, আমি ভুল করেছি, এই স্বীকারোক্তির মধ্যে যে অমল আত্মমর্যাদা, তাকে খেয়ে ফেলে অহংকারী অশিক্ষিত আত্মপক্ষ সমর্থনের বাতুলতা।’
‘কিংবা এই বাতুলতাও এক সত্য যা আমরা অন্ধকারে রাখতে স্বস্তি বোধ করি।’
‘তা বটে। বাতুলতা অসত্য হয় কী করে? বাতুলতা বাস্তব। তারই বৃহত্তর রূপ বৃহদাকার অপরাধে।’
‘নিজ অপরাধমনস্কতা গোপনের ফন্দি যদি বাতুলতা হয়, সেই সত্যাপলাপ কি আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রয়োজনীয় প্রতিরোধক্ষমতার পথ তৈরি করে?’
‘তাকে যদি তুমি প্রতিরোধক্ষমতার পথ বলো, ভুল হবে না। যার তাৎক্ষণিক অনুশোচনা আসে না, তার ওই প্রতিরোধক্ষমতা প্রবল। কিন্তু ধীরে ধীরে তা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অপরাধী যখন পাকড়াও হয়, প্রথম ধাক্কায় তার আত্মবিশ্বাসে আঘাত লাগবেই।’
‘যদি পাকা অপরাধী হয়? যদি হয় মিথ্যায় ওস্তাদ?’
‘তাদেরও আত্মবিশ্বাসে ধাক্কা লাগে, প্রকাশ করুক আর না করুক। ধৃত হলে যে বাস্তব প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সে যায়, পোড়খাওয়া না হলে তার চিন্তাপ্রক্রিয়া কিছুক্ষণের জন্য বিভ্রান্ত হবে। পুলিশ, থানা, জিজ্ঞাসাবাদ, স্বীকারোক্তির জন্য প্রহার, বিচারের নামে অনির্দিষ্টকাল ধরে আদালত গমন ও উকিলের জন্য অর্থব্যয়, জেলখানায় বসবাস ও সেখানকার অত্যাচার, ইত্যাদি জটিল, কঠিন, নির্মম, নিষ্ঠুর পথ অতিক্রম করতে করতে প্রতিরোধ বিশেষ বাকি থাকে না। মনে হয়, কেন করলাম? কী দরকার ছিল? এই তো সামান্য জীবন। অন্যায় অপরাধ না করেই দিব্য বেঁচে থাকা যায়। এই আর কী।’
‘সে আর ক’জনের মনে হয়?’
‘তাও বটে।’
‘তোমার কী মনে হয় বন্ধু?’
‘আমি কোনও অপরাধ করিনি। তাই আমার কোনও অনুশোচনা নেই।’
‘হ্যাঁ। তুমি আমাকে অনেকবার বলেছ সেই কথা।’
‘তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না? তুমি এর মধ্যেই সন্দেহবাদের ভিতরে প্রবেশ করেছ?’
‘না বন্ধু। আমার কর্তব্য, কয়েদিকৃত অপরাধ বিষয়ে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের ঠিক মধ্যবিন্দুতে অবস্থান করা।’
‘এর অর্থ কী?’
‘তুমি ও তোমার অপরাধসমূহ আমার চোখে একাকার হয় না। আমি কয়েদির বিচারক নই। আমি প্রহরী মাত্র।’
‘ঠিক, ঠিক বলেছ।’
‘তুমি বলো, বলো সেই কথা। অপরাধী ধরা পড়ে বিচারপ্রক্রিয়া পর্যন্ত চলতে চলতে নিজের জোর হারাতে থাকে?’
‘হারাবেই, এমন নয়। অপরাধমনস্তত্ত্ব বহুমুখী। এমন অপরাধীও বর্তমান, যে ধৃত হলে আরও জোরের সঙ্গে পরবর্তী কৃত্য বিষয়ে চিন্তা শুরু করবে।’
‘সংশোধনাগার অপরাধী মাত্রেরই শুদ্ধি ঘটায় না, আমি দেখতে পাই।’
‘তুমি বহুদর্শী। তবে সব রকমের দোষীদের একত্রিত করে আরও সবিস্তারে ভাবতে গেলে, এ কথাও বলা চলে, বিচারের জন্য অপেক্ষমাণ ওই সুদূর সারি, যেন মহাপথে ভিক্ষাপাত্র হাতে হতাশ বিধ্বস্ত মানুষের মিছিল। চোখ-মুখ ভাবলেশহীন, পঙক্তিতে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু কেন তা ভুলে গেছে, সত্যিই ভোলেনি, কিন্তু ভুলে থাকছে, কারণ তাদের আছে আরও বহু ভাবনা যা বিচার প্রার্থনার কুহকে ক্ষীণ, অপুষ্ট, অসম্পন্ন।’
‘আহা। তাদেরও ঘর-পরিবার আছে।’
‘ওই সুদীর্ঘ প্রতীক্ষাও কারাবাস।’
‘প্রকৃত অপরাধী হোক বা না হোক, বিচারপ্রার্থীর জন্য এই দিগন্তস্পর্শী লাইনে দাঁড়ানো শাস্তিভোগ।’
‘তখন অনুশোচনার রূপ বদলে যায়। নিরপরাধ অভিসম্পাত দেয় ঈশ্বরকে। দুর্ভাগ্য থেকে সৌভাগ্যের সিঁড়ি খুঁজে পাবার জন্য যাকে বিশ্বাস করার নয়, তার নির্দেশেও হয় একান্ত নির্ভর। এই দুর্দশা থেকে যেকোনও প্রকার নিষ্কৃতি কাম্য, এমনকী পলায়ন, যে দোষ সে করেনি তাকেই কবুল করে নেওয়া যাতে একরকম নিষ্পত্তি হয়। কিংবা ধৈর্য ও হতাশার অসহনীয় বিন্দুতে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত। গলায় ফাঁস দেওয়ার আগে কী ভাবে তারা? আমারই কেন এরকম হল, জগতে এত লোক থাকতে? কী ভাবে? যা লিখে যায় তা-ই কি? আর পারলাম না। ক্ষমা করো। কিংবা যে তার কপালে দুর্ভাগ্যের দগদগে ঘা করেছে, যার ওপর নিরন্তর নির্যাতনের ভনভনে মাছি উড়ে উড়ে এসে বসে, রসরক্ত চুষে খায়, জ্বালা-যন্ত্রণা ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে চলে, সেই দায়ভাগীর কথা মনে পড়ে, লিখে যায়, আমার মৃত্যুর জন্য সে দায়ী। ওঃ, ভাবো বন্ধু, নিজেকে নিজে হত্যা করার সময়ও যদি কেউ প্রিয়জনের কথা না ভাবে, ভাবে শত্রুর কথা, তার চেয়ে দুখী আর কে।’
‘অপেক্ষমাণের সারিতে অপরাধীর আচরণ অন্যতর কি?’
‘কী জানো, দোষ স্বীকার করলে বিচারের পথ হয় সংক্ষিপ্ত। না করলে যাত্রাপথ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়। তখন ওই প্রতিরোধক্ষমতার পরীক্ষা, ক্ষমতা ফুরোলে হয়তো অনুশোচনার পর্ব, অথবা যেভাবে মানুষ অপ্রয়োজনীয় স্বতোৎসারিত গাছ আগাছা বলে নির্মমভাবে কেটে ফেলে, সেভাবেই অনুশোচনার অনুবর্তী না হয়ে ভালো ও মন্দের ভেদাভেদজ্ঞানের সঙ্গে রফা করে নেয়। অবশেষে সংশোধনাগার থেকে বেরিয়ে আসে কারখানা থেকে বেরুনো বর্জ্য পদার্থের মতো শয়তান হৃদয়হীনেরা। বর্জ্য যেমন মেশে কল্যাণী নদীজলে, তেমনই।’
‘বন্ধু, তোমার কোনও অনুশোচনা নেই। জানতে ইচ্ছে হয় তোমার আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রক্রিয়া। তা কি বিবেকবান? নাকি বিবেকবিবর্জিত?’
‘আমাকে তুমি বিবেকহীন বলো?’
‘আমি সামান্য প্রহরী। আমি কিছুই জানি না। কিছুই বুঝি না। আমি শুধু জানি, এই কাজ। তুমি আমাকে বলেছ বন্ধু, আমি আপ্লুত হয়েছি।’
‘দক্ষিণের দেওয়াল, তুমি কি জানো না, কোনও অপরাধই নয় অপরাধ যদি তার পক্ষে যথার্থ ব্যাখ্যা, যুক্তি অথবা স্বপ্ন থাকে।’
‘ব্যাখ্যা বুঝলাম। যুক্তি অথবা স্বপ্ন, সে কীরকম?’
‘খুব সহজ। যা করেছি দেশের জন্য। যা করেছি ধর্মের জন্য। যা করেছি ঈশ্বরের আদেশে করেছি। আমি নিঃস্বার্থ। আত্মোৎসর্গ করেছি আমি।’
‘যে নিজেকে উৎসর্গ করেছে, সে কি ক্ষমতাসীন শাসকের দণ্ড গ্রহণ করে?’
‘গ্রহণ করে না, বরণ করে। কারাবাস, অত্যাচার, নিপীড়ন, দণ্ড সমস্তই বরণ করে বন্ধু, কারণ আত্মোৎসর্গের আদর্শ মানবের হৃদয় বদলে দেয়। তারা কৃতকর্ম অপরাধ গণ্য করে না, কর্তব্য বোধ করে। দণ্ডের রজ্জু অনায়াসে ফুলের মালার মতো গলে পরে। সুখের সঙ্গে পরে না। দুঃখের সঙ্গেও পরে না। আদর্শবাদী যখন মৃত্যু অনিবার্য জেনেও কর্তব্য স্বীকার করে, তার মন সাধারণ দুঃখ-সুখের মধ্যে থাকে না আর। চেনা জগতের নৈতিকতা ও আবেগ অতিক্রম করে যেতে হয়।’
‘তুমি কি তাদের কথা বলছ, যারা নিজের শরীরে বিস্ফোরক বেঁধে মৃত্যুচুম্বনের জন্য জড়িয়ে ধরে বধ্যদের?’
‘তারা এই আদর্শবাদীর দলে পড়ে। নিশ্চয়।’
‘এই পদ্ধতি যুক্তিসংগত মনে করো তুমি?’
‘প্রয়োজনের নিরিখে নিশ্চয় সংগত।’
‘সেই প্রয়োজন কি নিরপেক্ষ হতে পারে?’
‘কোনও প্রয়োজন নিরপেক্ষ হতে পারে না।’
‘আমি এক কয়েদিকে পেয়েছিলাম, যে দেশের এক গুরুত্বপূর্ণ সৌধ, সেখানকার বসবাসকারী সমেত ধ্বংস করতে এসে ধরা পড়েছিল।’
দক্ষিণের দেওয়াল আনমনে বলে যায়। বলতে বলতে একটি বিড়ি জ্বালায়। দু-টান দিল কি দিল না, অদূরবর্তী প্রহরী বিড়ির ভাগ নিতে এগিয়ে এল। দু-টান দিয়ে নিঃশেষিত বিড়ির অপেয় অংশ ফেলে দিয়ে বলল, ‘মাইরি, তোর ডিউটি আমার হলে ভালো হত।’
‘আমি দক্ষিণের দেওয়াল। ফিক্সড। তুই আমার মতো এক জায়গায় থেকে যা।’
‘না। এই ঠিক আছি।’
‘তাহলে সমস্যা কী?’
‘লোকটা, আমার সেলের নতুনটা, টোটাল বাইশটা খুন করেছে।’
‘খুনে লোক।’
‘লাস্ট শালার এক খানকিকে মেরে খালে ফেলে দিয়েছিল। ওতেই ধরা পড়েছে।’
‘ও খুনে, কাকে কখন কীভাবে কোতল করবে, ওর ব্যাপার। তোর অসুবিধা হয় কেন?’
‘শালার বাইশটা খুন।’
‘বাইশটা স্বীকার করেছে। আরও বেশি হতে পারে। তাতে কী? হননের সংখ্যার কাছে শাস্তির উপযুক্ত প্রয়োগ চিরকাল হেরে বসে থাকবে।’
‘লোকটার দৃষ্টি নজর করিস। তোর পেচ্ছাব পেয়ে যাবে।’
‘না। আমার পাবে না। তুই ক্যাবলাচোদা, ওর চোখে চোখ হাতে হাত রেখে বসে থাকিস নাকি?’
আরও কিছু ব্যক্তিগত সমস্যার কথা বলে সে চলে গেল।
প্রহরী দক্ষিণ পুনরায় বলতে লাগল সেই ছেলেটির কথা যে আদর্শ ও অত্যাচারের মধ্যে দোদুল্যমান।
‘আদর্শ ও অত্যাচার, নাকি আদর্শ ও অপরাধবোধ? অনুশোচনা?’
‘হয়তো সব। হয়তো কোনওটা নয়। শুধু সেই ভিনদেশি কয়েদি নিজের মৃত্যুর ছায়া দেখতে পেয়েছিল বলে খানিক উন্মাদ হয়ে ছিল।’
‘বহু অপরাধী আত্মকৃত অপরাধের ভার বইতে না পেরে উন্মাদ হয়ে যায়।’
‘শাস্তির পরিণতি সইতে পেরেও উন্মাদ হয় কত।’
‘যে নির্দোষ, অথচ দোষী সাব্যস্ত, তার পক্ষে মানসিক ভারসাম্য হারানো বিস্ময়কর নয়। ওই পরদেশি ঘাতক কি অপরাধসাধনে ছিল?’
‘ছিল।’
‘বেশ। বলে যাও।’
‘আদর্শের লক্ষ্য পূর্ণ করতে গিয়ে সে অনেক নির্দোষ মানুষকে হত্যা করে। সে যখন বিচারাধীন, আমি, এই দক্ষিণের দেওয়াল কয়েকদিন তার প্রহরায় নিযুক্ত ছিলাম। তোমাকে মিথ্যে বলব না, সে আমার অন্তর স্পর্শ করেছিল।’
‘কী করত সে?’
‘সে ছিল সন্ত্রাসবাদী। মাত্র একুশ বছরের তরুণ।’
‘তারুণ্যই তোমার অন্তরে কারুণ্যের কারক?’
‘অংশত সম্ভব। প্রথমদিকে সে সারাদিন গুম হয়ে থাকত।’
‘তারপর?’
‘সেই বন্দি কাঁদত। দেওয়ালে মাথা ঠুকত। বিচার শেষ হওয়ার আগেই যাতে সে নিজেকে খুন করে না ফেলে তার জন্য তাকে বেঁধে রাখা হল। শুধু খাবার সময় তার হাতের শেকল খুলে দেওয়া হত।’
‘আর?’
‘উদ্যত বন্দুকের সামনে সে স্নান করত, আহার করত, নিতান্ত অনিচ্ছায়। শৌচালয়েও তাকে নজরবন্দি থাকতে হয়। তাকে দেওয়া হত উচ্চমানের খাবার। কারণ বহু চক্রান্ত বিষয়ক তথ্য পাবার জন্য রাষ্ট্র তাকে কিছুকাল জীবিত ও সুস্থ চায়। প্রত্যেকদিন সে জেরাঘরে যায় আর ধ্বস্ত হয়ে ফিরে আসে। একটু একটু করে সে ফুরিয়ে আসছিল।’
‘আহা, তরুণ কি সুদর্শন?’
‘নিশ্চয়। আমার যেকোনও তারুণ্যই বড়ো সুন্দর মনে হয়।’
‘এইজন্যই তুমি দক্ষিণ। সার্থকনামা তুমি।’
‘একাকী, নিপীড়িত, ব্যথিত ও অসহায়, আর্তস্বরে বলত তার ওপর প্রযুক্ত অত্যাচারের কথা। শুধু আমিই সেসব শুনেছি।’
‘কেমন সেই অত্যাচার?’
‘গোপন তথ্য নিষ্কাশনের জন্য তার নাক ডুবিয়ে দেওয়া হল গরম চায়ের কাপে।’
‘আর?’
‘কাচের কাগজ চাপা দিয়ে ফাটিয়ে দেওয়া হয় নখ।’
‘আর?’
‘মুখে পুরে দেওয়া হয় গোটা গরম সেদ্ধ আলু।’
‘বাঃ, কতদিন আলুসেদ্ধ ভাত খাইনি।’
‘যেদিন তাকে উলটো করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, সেদিন সে আর তার কুঠুরিতে ফিরে আসেনি। তাকে হাসপাতালে যেতে হয়েছিল। ফিরে আসার পর ভেঙে পড়া কান্নার মধ্যে সে বলে ওঠে, ওরা আমাকে মেরে ফেলছে না কেন? আমি যা জানি, সব বলেছি। আসলে আমি কিছুই জানি না। ওরা বিশ্বাস করছে না কেন? মরতে ভয় পাই না আমি। কিন্তু এই অত্যাচার আর সহ্য করতে পারছি না। ওরা বোঝে না কেন, যাদের হয়ে কাজ করেছি তাদের কাউকে আমি চিনি না।’
‘সন্ত্রাসবাদীরা মরতে মরতেও মিথ্যে বলে। ওদের মিথ্যাচারের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।’
‘কিংবা এক একুশবর্ষীয় তরুণ হয়তো সত্য বলেছিল।’
‘একুশ হোক আর এগারো, সন্ত্রাসবাদী মানেই মিথ্যুক ও ঘাতক।’
‘তার ঘরে খাবার নেই, পরিবারে শিশু, নারী, বৃদ্ধদের চিকিৎসার পয়সা নেই।’
‘না থাকলেই হত্যা ও ত্রসনের পথ নিতে হবে?’
‘নিজের ঘর নেই, জমি নেই, লেখাপড়ার সুযোগ নেই, রোজগারের পথ নেই, এমন হাজার নেইয়ের মাঝখানে প্রতিদিন গুচ্ছমূল কন্দের মতো গজিয়ে ওঠে অগণিত অস্তিত্ব।’
‘ওঃ, দক্ষিণ, প্রিয় দক্ষিণ, সন্ত্রাসের কারবারি নিয়ে আমার অভিজ্ঞতা তুমি জানো না। ওরা তোমার মাথা খেয়ে ফেলতে পারে। যতই নিরেট মাথা হোক, চিবিয়ে খেয়ে ফেলে।’
‘ওদের খিদে পায়। বন্ধু। খিদের চেয়ে দুঃসহ আর কী হতে পারে? বরফে ঢাকা দুরন্ত শীতের উন্মত্ত বায়ু ভাঙা ঘরের ফোঁকর গলে ঢুকে পড়ে অপর্যাপ্ত আচ্ছাদন পরাস্ত করে।’
‘আহা।’
‘দারিদ্র্য। হতাশা। দীর্ণজীর্ণ নিঃস্বপ্ন জীবনে যদি কেউ বলে অনেক অনেক টাকা পাবে। তোমার পরিবারের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার মতো ঢের টাকা। বিনিময়ে? তোমাকে আদর্শে বিশ্বাস করতে হবে, যা করছ ধর্মের জন্য। সে তৎক্ষণাৎ বিশ্বাস করে। বিশ্বাস বই তো কিছু নয়। বিশ্বাস ছাড়া আর কী আছে?’
‘বিশ্বাস? নাকি লোভ?’
‘লোভ? হ্যাঁ। হতে পারে। জীবনের লোভ। বেঁচে থাকার লোভ।’
‘লোভ ও আদর্শ একত্রে পরিবেশন করে যারা, কী বলল সেই তরুণকে?’
‘তারা বলল, তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে, ঈশ্বর তোমাকে, তোমার মতো আরও কয়েকজনকে, তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য এই পৃথিবীত পাঠিয়েছেন। ঈশ্বরের ইচ্ছাই তোমার ইচ্ছা করে তুলতে হবে।’
‘শুনে কী বলেছিল সেই তরুণ?’
‘বলেছিল, আমার ইচ্ছা হয়, সপরিবারে, গ্রামের সকলকে সঙ্গী করে, আমাদের এই অত্যাশ্চর্য সুন্দর ভূখণ্ড ও তার অধিবাসীদের জীবন নিরাপদ, সম্পৎশালী, শিক্ষিত ও সম্মানজনক করতে পারতাম যদি। কিন্তু ঈশ্বর আমাকে সেই সুযোগ কেন দিচ্ছেন না?’
‘কী বলল তার নেতা?’
‘বলল, ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করো, তিনিও তোমার বাসনা পূর্ণ করবেন।’
‘তারপর?’
‘সেই তরুণ জিজ্ঞেস করল, ঈশ্বরের ইচ্ছা কী?’
‘নেতা বলল, শত্রু শাতন করতে হবে। তা-ই তো।’
‘তা-ই বলল বটে। তখন সেই তরুণ বলল, না আমি কারো ক্ষতি করেছি, না কেউ আমার ক্ষতি করেছে। তাহলে আমার শত্রু থাকে কী করে? কে আমার শত্রু? আমার গ্রামে কাউকেই আমার শত্রু মনে হয় না।’
‘বেশ, বেশ।’
‘তখন সেই নেতা বলল, শত্রু অনেকরকম হতে পারে। ঈশ্বর জীবনযাপনের যে বিধান দিয়েছেন, যারা তার বিরুদ্ধাচার করে, তারাই শত্রু। তরুণ বলেছিল, কার শত্রু তারা? ঈশ্বরের শত্রু হওয়ার ক্ষমতা কার? সেই নেতা তখন গর্জন করে বলে, যা বলছি তা করো। বসে বসে তোমার প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমার কাজ নয়। ঈশ্বর আমার কাছে পাঠিয়েছেন তোমাকে। তুমি যদি এই সুযোগ গ্রহণ না করো, ঈশ্বর ক্রুদ্ধ হবেন। অজন্মা, অতিমারী বা পশুরোগে উজাড় হয়ে যাবে তোমাদের গ্রাম। আর যদি যা বলছি, তাতে সম্মত থাকো, জীবনে সুখই সুখ, মজাই মজা।’
‘তরুণ রাজি হয়ে গেল? গাঁয়ে ফিরে জুটিয়ে আনল আরও কতক স্বপ্নের চাবুক হাঁকানো তরুণ? তারা সকলেই লোভী ও ঘাতক হয়ে গেল?’
‘তরুণ জিজ্ঞেস করেছিল, তাকে কী করতে হবে। সেই নেতা পরিষ্কার বলে, শত্রু নিকেশ করতে হবে। আগেই তো বললাম। আমাদের অগণিত শত্রু। তাই গণহত্যা দ্রুত বৈরী নাশ করবে। পারবে করতে?’
‘কী বলল? তরুণ কী বলল? কেমন মাথা চিবিয়ে খায় ওরা, দেখছ তো?’
‘তরুণ দ্বিধান্বিত ছিল। বলল, হত্যা করা পাপ। হয়তো পারব না। একটাও মোরগও আমি কখনো মারিনি।’
‘অতঃপর?’
‘সেই নেতা ফের বলল, শেষ সুযোগ, ভেবে দেখো, পরিবার সুখে-সম্পদে থাকবে। গ্রাম থেকে আরও কয়েকজন যদি আনতে পারো, তবে সারা গাঁ হয়ে উঠবে বিত্তশালী।’
‘তরুণের চোখ ধাঁধিয়ে দিল স্বপ্নের চাবুক।’
‘সে বার বার জিজ্ঞেস করল, পরিবার সুখে থাকবে তো? কোনও কষ্ট পেতে হবে না তো তাদের? নেতা সমূহ অধিগ্রহণ সম্ভাবনায় উৎসাহের সঙ্গে বলল, ধর্মের নামে শপথ, থাকবে। যা করছ, ধর্মের জন্য। এই কাজে তুমি যেমন শত্রু হত্যা করে পুণ্য অর্জন করবে, তেমন শত্রুকে দুর্বল ভাবার কারণ নেই, তারা বর্বর, তোমাকে হত্যা করতে পারে। সেই মৃত্যু বীরের মৃত্যু। সেই মৃত্যু সারাজীবনের সঞ্চিত পুণ্যের সমান। তুমি অক্ষয় স্বর্গবাস করবে। ধর্মের জন্য নিজেকে বলি দাও, ধর্ম তোমাকে অমর শহিদ করে রাখবে। পরিবারে তোমার উত্তরসূরি দুধে-ভাতে থাকবে, মাথা উঁচু করে বলবে, ওই উনি ছিলেন মহান। তোমার অর্থহীন জীবন অর্থপূর্ণ করে দিতে পারে কে? ধর্ম। ধর্ম কী? ঈশ্বরের বাণী ও নির্দেশিত পথ। তুমি-আমি তাঁর ইচ্ছার অধীন।’
‘বেশ। আমার চেনাপথেই এগোচ্ছে তোমার কাহিনি। তা-ই হোক। সে রাজি। রাজি? মরতেও রাজি?’
‘মরা? বিশ্বাসের মধ্যে নিজের মরে যাওয়ার কথাও আছে নাকি? তার গ্রামের বন্ধুরা জিজ্ঞেস করেছিল। একজন বলল, অনেকেই এই কাজ করে বড়োলোক হয়ে গেছে। আর-একজন বলল, মরতে একদিন হবেই, তাহলে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করেই মরা যাক, পরিবার ভালো থাকবে। সুতরাং তারা হত্যাকারী হওয়া মনস্থ করল।’
‘মারতে যাওয়া আর মরতে যাওয়া সবসময় একসঙ্গে চলে।’
‘কিন্তু যে পরিবারের ভালো থাকার জন্য এমন সংকল্প, যে পরিবারের স্নেহ-ভালোবাসা জীবনের একমাত্র অবলম্বন, সেইসব ফিরে পাবার জন্য, তারা সত্যি ভালো আছে দেখার জন্য যদি বেঁচে না থাকে, তাহলে লাভ কী?’
‘দেখা যায় বইকী, নিশ্চয় দেখা যায়, কারণ আদর্শায়িত হত্যার সংকল্প ঈশ্বরের আদেশ, সেই আদেশ পালন করলে তুমি স্বর্গলাভ করবে, যেখান থেকে চাইলেই পরিবারকে দেখা যায়।’
‘এ নিয়ে কোনও সংশয় থাকে না যে স্বর্গ সেই চূড়ান্ত লক্ষ্য যেখানে কামনা অনির্বাণ কিন্তু বাসনার কোনও স্থান নেই। কেননা বাসনা রচিত হওয়ার মতো কোনও শূন্য পরিসর থাকে না সেখানে। অতএব এক নিকৃষ্ট অবস্থান থেকে স্বর্গলাভের আকর্ষণে সে প্রথমে আদর্শ বিষয়ক শপথ নেয়, মারব নয়তো মরব। তার ওপর স্বয়ং ঈশ্বর যে কর্তব্যভার অর্পণ করেছেন, আরও কোটি তরুণ থাকা সত্ত্বেও এই পবিত্র কর্মসাধনে তাকেই নিযুক্ত করেছেন, এই বিশ্বাসেও সে অবিচলিত থাকার প্রতিজ্ঞা নেয়। তবে হত্যা সত্যি পবিত্র কি না এ বিষয়ে সে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল।’
‘নিশ্চয় পবিত্র। হত্যার উদ্দেশ্য দেখে বুঝতে হবে তা পাপ না পুণ্য। লোকে কি বলি দেয় না? পশুপক্ষী? ঈশ্বর চান বলেই তো দেয়।’
‘পশুপক্ষী বলি, আর নরবলি কি এক?’
‘ঈশ্বর চাইলে এক। দেখো না কি, পাহাড়ের ধস কত গ্রাম ধ্বংস করে দেয়? বন্যায় ডুবে মরে কত মানুষ? খরায় শুকিয়ে মরে? ভূমিকম্পে? পুণ্যার্থে পুণ্যধামে যাত্রা করেও দুর্ঘটনায় মারা যায়? আর কিছু না হলেও, পুণ্যকামীর পায়ে পিষে মরে যায় কত পুণ্যার্থী? ঈশ্বর চান বলেই এমন ঘটে। পুণ্যমানের দ্বারা পুণ্যবানের পদদলন ও হত্যা। মন্দিরের ভিতর, দরিদ্র অসহায় বালিকাকে বেঁধে দিনের পর দিন পুরোহিত তাকে ধর্ষণ করে, তার সঙ্গীরাও করে, চূড়ান্ত নির্যাতনের পর হত্যা করে ও কলার খোসার মতো রাস্তায় ফেলে দেয়। সে-ও কি ঈশ্বরের ইচ্ছা নয়?’
‘দ্বিধা থেকে সংকল্পে, জিজ্ঞাসা থেকে স্বর্গলাভের স্বপ্নে স্থিত হওয়ার পথে, কারাগারে নিক্ষিপ্ত জীবনে অত্যাচারের কোনও বর্ণনা ছিল না তার কাছে। সে মরে যেতে পারে, এই তথ্য দিয়েছিল, কিন্তু যদি ধরা পড়ে যায়, শত্রুরা কীভাবে তার বিচার করবে, এই কথা কখনো বলেনি কেউ। বলেনি, তার পশ্চাদ্দেশে ঢুকিয়ে দেওয়া হতে পারে জীবন্ত সাপের বাচ্চা। তার শিশ্নে লাগিয়ে দেওয়া হতে পারে রক্তপ জোঁক। তবে, তাকে সতর্ক করা হয়েছিল বটে, কাউকে, কোথাও, এই প্রশিক্ষণকেন্দ্র সম্পর্কে কোনও তথ্য দিলে তার পরিবার বলে কিছু থাকবে না।’
‘সে-ও ঈশ্বরের আদেশ, বলেছে নিশ্চয়?’
‘অর্থলোভ, সুখ ও নিরাপত্তার বিনিময়ে কিনেছিল যে আদর্শ ও বিশ্বাস, তা-ই দিয়েই সে শেষ পর্যন্ত শান্তভাবে ফাঁসির দড়ি গলায় পরেছিল। কিন্তু দৈহিক ও মানসিক নির্যাতনের অজ্ঞাত পথ পেরোতে সে বার বার বলেছে, এর চেয়ে ভালো তার মুণ্ড কেটে নেওয়া। কিংবা গুলি করে মারা। ”কেন আমি ধরা পড়ে গেলাম? কেন মরে গেলাম না? কেন? কেন? কেন?” এই বলে মাথা খুঁড়ত সে।’
‘সে তোমার হৃদয়ে বাস করে, বুঝতে পারলাম।’
‘তাহলে বলো,’ দক্ষিণের দেওয়াল প্রশ্ন করে, ‘টাকা দিয়ে আদর্শ খরিদ করা যায়, ঠিক যেমন মেথ, কোকেইন, ক্রিস্টাল, মদ।’
‘মেথ? মেথ্যাম্ফেটামাইন? আর আদর্শ? হ্যাঁ। মিল আছে। দুইই টাকা দিয়ে কেনা যায়। কিনতে হয়। বা, একটু রেখেঢেকে বলা ভালো, আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য, প্রবহণের জন্য অর্থব্যয় করতেই হয়। আদর্শেও প্রাণ দিতে হয়, মেথ বা যেকোনও অপরিমিত অভ্যাস মৃত্যুর কারণ হতে পারে। কিন্তু কাঁচা নর্দমার জলে যে সর পড়ে, তার সঙ্গে দুধের সর কি এক করবে তুমি? একজনকে, বা ধরো, একশো অভুক্ত মানুষের মধ্যে দশজনকে এক সপ্তাহ পেট ভরে খাওয়ানোর পর যদি দাবি করা হয়, দেশে দারিদ্র্য বলে কিছু নেই, তা যেমন কোনও নির্দিষ্ট আদর্শ বা কল্যাণকর লক্ষ্য প্রতিষ্ঠা করে না, তেমনই ওই ছেলেটির পরিণতি। সে একা দরিদ্র ছিল না, তার প্রতিবেশী, তার গ্রাম, তার রাজ্য, দেশ সর্বত্র অগণিত অভুক্ত, কর্মহীন, নিরাপত্তাহীন মানুষ। তার আদর্শগ্রহণের বিনিময় ক্ষুদ্র স্বার্থের অন্বেষণ। যা করেছে ধর্মের জন্য, যা করেছে পরিবারের জন্য, যা করেছে গ্রামের জন্য, ঈশ্বরের নির্বাচন যে সে নিজে, এই বার্তা ঈশ্বর স্বয়ং তাকে না দিয়ে কেন একজন দালাল পাঠালেন, এই প্রশ্ন সে করতেই চায়নি।’
‘হয়তো এই প্রশ্ন সে করতে শেখেনি। সাপের কামড়ে মৃত্যু হলে যারা বলে, মা মনসা দয়া করেছে, তারা ঈশ্বরের দালালদের প্রায় ঈশ্বর বলেই মানে, কারণ, চরম গরিব মানুষ সেই দালালরূপী ঈশ্বরের ওপরেই নির্ভর। তাদের কাছে আদর্শ বিক্রয় অতি সহজ, এটাই স্বাভাবিক।’
‘তুমি কি বলতে চাও, আদর্শের নামে, ঈশ্বরের মিথ্যা নির্দেশ, স্বর্গের ভুয়ো স্বপ্ন ও পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তার লোভ দেখিয়ে ওই ছেলেটিকে ব্যবহার করা হয়েছে?’
‘হ্যাঁ, ব্যবহার। ওই ধ্বংস ও হত্যা যদি এতই পবিত্র কর্তব্য, ঈশ্বরের দূতগণ অন্তরালে না থেকে প্রকাশ্য যুদ্ধে নামে না কেন?’
‘কোনও যুদ্ধই প্রকাশ্য নয় বলে।’
‘সে কীরকম?’
‘বন্ধু, যুদ্ধ হয় অন্তরালে, ঠান্ডা ঘরে হুইস্কি পান করতে করতে যুদ্ধ করে আধুনিক পৃথিবী। বাইরে যা কিছু দেখা যায়, গুলি, বোমা, মিসাইল, মাইন, ট্যাঙ্ক ইত্যাদি ধ্বংসের উপায় মাত্র।’
‘যারা বীর সেনানী, তারা কি দেশের জন্য প্রাণ দেয় না? তারা কি আদর্শবাদী নয়?’
‘অবশ্যই আদর্শবাদী। তবে আদর্শ জিনিসটা আপাতভাবে যত সহজ সরল নিটোল নির্মল বলে ভাবতে ভালো লাগে, আদপে তা নয়। ওই তরুণের জীবন ও মৃত্যু এই ধারণা দেয়, হৃদয়ে আদর্শ গেঁথে দেওয়া এক প্রক্রিয়া। দেশের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য, ক্ষমতার জন্য, কত রকমের যুদ্ধ হয় তুমি জানো না।’
‘আমি সামান্য প্রহরী, আমারও কিছু আদর্শ আছে। সে তো কেউ গেঁথে দেয়নি।’
‘দিয়েছে। নিঃশব্দে গেঁথে দিয়েছে তোমার সমাজ।’
‘ওই ছেলেটি অত্যাচারে প্রায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল। প্রলাপের মতো খেদোক্তি করত সে। ঠিক অনুশোচনা নয়, দুর্বোধ্য যন্ত্রণার অজানিত ভাষ্য, যা আমি অনুশোচনা বলেই ভেবেছি। তার কাছে ওই আদর্শ বিক্রয় করে যদি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে গেঁথে দেওয়া যেত, তার অনুশোচনা হত না?’
‘হতে পারে। আবার না হতেও পারে। কারণ চিন্তন হল নদীর মতো। জোর করে তুমি তার বাঁক ঘুরিয়ে দিতে পারো, কিন্তু আপন শক্তিতে তা ভেঙে পথ করে নিতে পারে।’
‘অর্থাৎ আজ যা আদর্শ বলে মনে হচ্ছে, কাল তা অপকর্ম বোধ হতে পারে। অনুশোচনাও জন্মাতে পারে?’
‘ঠিক।’
‘কিন্তু ধরো, তার কাছে তথ্য আদায়ে সফল হতে পারেনি বলে যে অত্যাচার, তা কি অপরাধ নয়? কোন আদর্শে তারা সে কাজ করে? রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা যেহেতু তা করে, তাকে রাষ্ট্রকৃত অপরাধ বলা চলে না?’
‘তারা আদর্শে অত্যাচার করেনি, আদর্শের পথ রক্ষা করার কর্তব্যে ওই উপায় নিয়েছে।’
‘কী সেই আদর্শ?’
‘দেশ রক্ষা করা। দেশের শত্রু সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহ, তার উদ্দেশ্য, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ইত্যাদি যত বেশি জানা যায়, দেশের জনগণ তত বেশি সুরক্ষিত থাকে।’
‘সেই তরুণকে হত্যা করে দেশ কতখানি নিরাপদ হল?’
‘তোমাকে বলেছি, আদর্শ সরল বস্তু নয়। ওই তরুণকে তুমি কাছ থেকে দেখেছ, তার বিলাপ, প্রলাপ, তার রূপ ও যন্ত্রণা তোমাকে তার প্রতি সহানুভূতিশীল করেছে। কিন্তু সে তোমার আমার দেশের কত নিরপরাধ হত্যা করেছে। কত পরিবার অসহায়, বিষাদাচ্ছন্ন, প্রিয়জন হারানোর বেদনায় কাতর। ওই তরুণ যেমন তার দারিদ্র্যের জন্য দায়ী নয়, ওই প্রাণ হারানো নাগরিকগণও নয়, তবে কেন এই হত্যা? কেন দেশ ওই তরুণের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে? সে তো এক্ষেত্রে এক সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী হননকামী আদর্শের প্রতিনিধি। গণহত্যা করে সে যে গণবিক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, রাষ্ট্রকে তা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে, রাষ্ট্র তাকে ক্ষমা করতে পারে না।’
‘সকলেই এই হত্যা, এই তরুণের মৃত্যুদণ্ড মেনে নিতে পারেনি।’
‘একশো কুড়ি কোটি নাগরিকের দেশে কোনও বিষয়ে সার্বিক ঐকমত্য সম্ভব নয়।’
‘তা বটে।’
‘যদি ছেলেটি ওদের, ওই অত্যাচারীদের একজনকে বন্দি করে আপন ধর্মযোদ্ধাদের ডেরায় নিয়ে যেতে পারত, সেখানেও একই প্রক্রিয়া চলত। এমনকী আরও বীভৎস, আরও ভয়ংকর, আরও সুদূরপ্রসারী সন্ত্রাস। অপরাধই বলো আর সুকৃতি, সমস্ত কিছু বহু মাত্রায় ব্যাখ্যা করা যায়। নদীর মতো।’
‘এই তো একবার নদীর উপমা দিয়েছ।’
‘আবার দিলে আপত্তি আছে? নদীবাঁধ দেওয়া জলাধার যেমন আবাদি ভূমির জলসেচ নিশ্চিত করে, জলবিদ্যুৎ দিয়ে অন্ধকারে আলো জ্বালে, তেমনই জলাধার নদীবাঁধ লঙ্ঘন করে বন্যায় ঘর ভাসিয়ে দেয়। ওই জলাধারের জন্য নদীর অপরাপর নির্ভরশীল ভাগীদার বঞ্চিত হতে থাকে। তাহলে নদী বন্ধু, না শত্রু? বাঁধ জরুরি, না অর্থহীন? জলাধার নির্মাণের আদেশ দিয়েছে যে রাষ্ট্রশক্তি, সে জনগণের মঙ্গল চায়, নাকি সে কোনও ফন্দিবাজ?’
‘চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অসম্ভব। কিন্তু বন্ধু, অনেক আগে তোমায় যে প্রশ্ন করেছিলাম, তার জবাব তুমি এড়িয়ে গিয়েছ।’
‘তুমি আমার একমাত্র বন্ধু, তোমার কাছে কী লুকোব যে এড়িয়ে যাব? কথা বলতে বলতে প্রসঙ্গান্তরে চলে যাই আর কী। অনুশোচনার কথা যদি বলো, তবে এই পরিস্থিতিতে নিজেকে নিয়ে আসার জন্য অনুশোচনা হয়। আমি অপরাধ করিনি, হঠকারিতা করেছি, এই শোচনা।’
‘সে কেমন?’
‘আমি সময় নিয়ে, সুপরিকল্পিত উপায়ে, লোকটাকে মেরে ফেলতে পারতাম। কেউ আমার কিছুই করতে পারত না। আমার উত্তরাকে আমার আশ্রয় থেকে কেউ সরিয়ে নিতে পারত না। সেই অবিমৃশ্যকারী হননের জন্য এই কারাবাস, যা আমাকে তার সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত করেছে। আমি তাকে ভালোবেসেছি। আমার প্রথম প্রেম ছিল আমার দেশ। সে আসার পর বুঝলাম, দেশ ও আমি যে প্রেমবন্ধনে সংযুক্ত, তার সংজ্ঞা আর এই ভালোবাসা ভিন্নার্থক। আমার জীবনের একমাত্র ভালোবাসা, সেই প্রেমপথে যে বাধাই আসুক, আমি ভেঙে ফেলতে চাইব, যে বাধা হয়ে দাঁড়াবে, তাকে খুন করে ফেলব। সেগুলোর জন্য আমার এতটুকু অপরাধবোধ নেই। আমি অপরাধ করিনি। ভুল ভুল ভুল করেছি সাক্ষ্যপ্রমাণ রেখে খুন করে। অনুশোচনা হয় ওই অবিমৃশ্যকারিতার জন্য। বোকার মতো। নিরেট নির্বুদ্ধির মতো। অথচ আমি প্রশিক্ষিত, ঠান্ডা মাথায় হত্যার জন্য প্রশিক্ষিত। দেশপ্রেমের আদর্শে, প্রয়োজনে, গণহত্যার জন্য গড়েপিটে নেওয়া একজন মানুষ।’
‘কী বলছ?’
‘হ্যাঁ, যা বলছিলাম। বোকা আমি। অথচ আমি বোকা নই। প্রেম মানুষকে বোকা করে দিতে পারে বলে শুনি, সে ব্যাপারে কিছু জানা আছে?’
‘আমিও শুনেছি। বোধহয় কথাটা ঠিক। আমার মনে হয় প্রেম, আদর্শ, ক্ষমতা, লোভ মানুষকে মোহাবিষ্ট রাখে। মোহ উন্মত্ততা। উন্মাদনা বুদ্ধিভ্রংশকারী।’
‘না না। প্রেম মোহ হতে পারে না। না। তুমি অন্তত প্রেমকে মোহ বলতে পারো না কিছুতেই।’
‘আমি কিন্তু ভালোবাসা বলিনি। প্রেম মোহ। ভালোবাসা মোহমুক্ত।’
‘ঠিক। এইবারে ঠিক বলেছ। আমি তাকে প্রেম করেছিলাম। কবে সেই প্রেম ভালোবাসা হয়ে গেছে। আর আমার কোনও মোহ নেই। দেশের জন্য যে আদর্শ গ্রহণ করেছিলাম, তার কর্তব্যভার আমাকে ছেড়ে গেছে। আমারও তাকে প্রয়োজন নেই। যাক।’
‘তাহলে? এইবার?’
‘আমি শুধু চাই, পশ্চিমের দেওয়াল ভেঙে বেরিয়ে পড়ব একদিন। মুক্তি। ওই যে ওপরের জানালা দিয়ে চিতা থেকে ধোঁয়া উঠে আসে, তার কাছে সারাদিন কত খবর। তাল রাখতে পারি না। দুনিয়া দ্রুত বদলে যাচ্ছে। চিতাকাঠ ছেড়ে বিদ্যুৎচুল্লির জন্য অপেক্ষা করে মৃতদের লাইন। মৃতদেহ পচে ফুলে ওঠে। গন্ধ ঢালে। কিন্তু শোকার্তের অনুভবে যে পচন লাগে, তাকে চাপা দেবে কোন অগুরু? আমি জানি অন্তরে পচনের গন্ধ।’
‘সেইসব ধুয়েমুছে ফেলতে হয়।’
‘সেইসব ধুয়ে ফেলতে এই ঘরের বাইরে তার কাছে যাওয়া ছাড়া আর কোনও কিছুই চাওয়ার নেই আমার। বাকি পৃথিবীর কিছুই আমি বুঝি না।’
‘বোঝো না বলে কি ভয়? কেন বোঝো না?’
‘বুঝি না, কারণ, প্রতিনিয়ত যে পরিবর্তন বিশ্বের, তার খবর রাখতে একদিন আমি ভুলে গেলাম। আমার শেকল, বেড়ি, আমার দেওয়াল ও ঘুলঘুলি, আমার শয্যার কীট ও বালিশের শ্যাওলা, আমার মুক্তির উপাসনায় ঘোর ব্যস্ত হয়ে গেলাম। কিন্তু, আমি তাতে ভয় পাই না। কিছুই ভয় পাই না।’
‘তোমার কাছে এই আমার প্রত্যাশা। ভয় যেন না পাও তুমি। ভয় পাওয়া খুব লজ্জাজনক।’
‘মানুষ মানুষকে ভয় দেখাতে পছন্দ করে। তবে তুমি ভেবো না। আমার আর কোনও ভয় নেই। এখান থেকে ছাড়া পেলেই আমি মুক্ত। হ্যাঁ। একেবারে মুক্ত। যাবজ্জীবন কারাবাস শেষ হয় না কি?’
‘সবকিছুই একদিন না একদিন শেষ হয় বন্ধু।’
‘ঠিক। ঠিক বলেছ।’
দক্ষিণের দেওয়াল কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল, ‘তাহলে এখন তোমার মুক্তি জেলখানা থেকে বেরুনোর অপেক্ষায়?’
‘আমি রোজ তার জন্য একটু একটু করে তৈরি হচ্ছি।’
‘আমার মুক্তি ঠিক কীরকম, সেটাই এখনও বোঝা হল না। যখন ছোটো ছিলাম, স্কুলে পড়তাম, পড়ার চেয়ে খেলা লাগত ভালো, কিন্তু খেলার চেয়ে পড়তেই বাধ্য ছিলাম বেশি। মনে হত, স্কুল পেরোলেই মুক্তি। বিড়ি ফুঁকে আর আড্ডাবাজি করে কলেজের দু-তিন বছর শেষ হয়ে গেল। যে বন্ধুদের একদিন না দেখলে রাতে ঘুম আসে না, তারা সবাই গেল ছড়িয়ে। যদি কখনো দেখা হয়, কেউ হতাশায় নুয়ে পড়ে এক ছিলিম তামাক খেতে ভুলে যায়, কেউ সাফল্যের অহংকারে চিৎকার করে বলে, চলে আয় একদিন, বিদেশি মাল আছে, খাওয়াব। ছিলিমের সুস্বাদু আগুন অভিমানী কিশোরীর চিতার মতো নিভে আসে। কলেজের গেটের সামনে একা একা দাঁড়িয়ে মনে হল, আমি কখনো আদর্শের কথা ভাবিনি, কলেজে কেউ রাজনৈতিক মতবাদের জ্ঞান দিতে এলে গাঁজার ধোঁয়া একমুখ ছেড়ে উড়িয়ে দিয়েছি। লেখাপড়া যেটুকু, তার পেছনে মা-বাবাকে সন্তুষ্ট রাখাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। বুঝলাম, কত নগণ্য আমি।’
‘তুমি কারাপ্রহরী, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তারক্ষী, বুক দিয়ে অপরাধী সামাল দাও, তুমি নগণ্য হও কী করে?’
‘তুমি বন্ধু, তাই আমাকে গণ্য করো। আসলে আমি সোজা দাঁড়িয়ে থাকা দেওয়াল বই কিছুই নই। নিজের তুচ্ছতা বুঝতে পেরে, একটা জলভরা দিঘি যদি শূন্য করে দেওয়া যায়, ওই ক্লেদাক্ত গর্ভ থেকে যেমন নিরুচ্চার হাহাকার ওঠে, আমার মধ্যে তা-ই উপস্থিত হল। মনে হতে লাগল একটা জীবিকা আঁকড়ানো ছাড়া আমার মুক্তি নেই। যে যা বলল, তা-ই করতে করতে এই চাকরি।’
‘নিশ্চয়। তুমি মুক্ত। তুমি নিজেই তার ঘোষণা করেছ। তোমার কর্তব্যই তোমার মুক্তি।’
‘যারা বেকার থেকে গেছে তারা বলল, তুমি তো ভাগ্যবান, একেবারে লগনচাঁদা। চাকরি জোটালে, তাও সরকারি।’
‘সরকারি চাকরির প্রতি ঈর্ষা আছে বটে তাদের, যারা সেই বস্তু অধিকার করতে ব্যর্থ হয়েছে।’
‘প্রথমে আমারও নিজেকে ভাগ্যবান মনে হয়েছিল। মাস গেলে টাকা পাই, বেতন এবং উপরির লুকোনো খাম। জেলখানায় সব কর্তা ও কর্মী তার হকদার। কখনো বেতনের চেয়ে উপরি বেশি পাই। সংসার সচ্ছল। ওই খাম এমনই স্বতঃপ্রতিষ্ঠ, সমান্তরাল আর্থিক কাঠামো যে দুর্নীতি, সে কথা কখনো ভাবিনি। নিজেকে মনে হয় অপরাধীদের মধ্যে একজন পবিত্র মানুষ।’
‘তুমি অবশ্যই পবিত্র দক্ষিণের দেওয়াল। কারণ একমাত্র পবিত্রহৃদয় আমার বন্ধু হতে পারে।’
‘একদিন হল কী, প্রহরীদের পাণ্ডা ডেকে হাতে একখানা প্যাকেট ধরিয়ে বলল, ”তোর তো ২০-র সেলে ডিউটি? ওখানে ১২২ নম্বরের হাতে এটা দিবি। কেউ যেন জানতে না পারে। আবার ফেরত আনবি। কাউকে বললে মাইরি পায়খানায় ডিউটি করিয়ে দেব। টুকটুকে চেহারা নিয়ে দাঁড়াবি আর হুমদো বাঞ্চোতগুলো ধরে চোদন দেবে।’
‘জেলখানার মধ্যে জেলখানা।’
‘ভাই, সেইদিন, এক মুহূর্তে আমি হয়ে গেলাম নিষ্পাপ প্রহরী থেকে পাপীদের টফি সাপ্লায়ার। অন্যতর পাপাচারী।’
‘পাপ কী, আর পুণ্যই বা কী?’
‘কারারক্ষী হয়ে নিজের মধ্যে দেশসেবার পবিত্র আদর্শবোধ যতটুকু শ্যাওলা ফেলেছিল, হুমকির ব্লিচিং পাউডারে সব খসে গেল।’
‘কচি বয়স ছিল তো, পশ্চাদ্দেশের মায়া হওয়ার কথাই। ভয় তো আরও বেশি। হেহ হেহ হেহ।’
‘বদলির চাকরি। এই জেল থেকে ওই জেল, সব জায়গায় কোনও শক্তিমানের আদেশ, মোলায়েম খিস্তি আর প্রহরার নামে দাগি দুর্ধর্ষ পাষণ্ড লোকগুলোর খিদমত খাটতে খাটতে আমি একখানা দেওয়ালই হয়ে গেলাম অবশেষে। হিলহিলে ঘিনঘিনে। কিন্তু সামান্য, তুচ্ছ। কারাগারের চারপাশে ওই কেমন বিশাল শক্তিমান প্রাচীর, তাদের পায়ের ধুলোর মতো। যখনই ওদিকে তাকাই, মনে হয় কত সামান্য আমি। কত হীন। এই হীনমন্যতা থেকে মুক্তি নেই।’
‘তবে দেখছি তুমি মুক্তমানব নও।’
‘এক অর্থে মুক্ত। কারণ আমি কিছুই চাই না।’
‘কেন? হীনমন্যতা থেকে মুক্তি? চাও না?’
‘না। চেয়ে কী লাভ? যাবে না। আমার নগণ্যতা থেকে পালাবার ক্ষমতা নেই আমার।’
‘এত সহজে পরাস্ত হবে?’
‘পরাজয় নয়। আত্মানুসন্ধান। তুমি কী, কতখানি, বুঝতে পারলে বাসনার অবসান হয়। মুক্তির বাসনাও তো বন্ধন।’
‘হীনমন্যতা বন্ধন নয়?’
‘না। আমি জানি আমার হীনতাবোধ আছে।’
‘নিজেকেই নিজে ঠকাচ্ছ তুমি। তুমিও আমারই মতো মুক্তিসন্ধানী বন্ধু।’
‘ধরা যখন পড়েই গেছি, তখন বলি, কীসের থেকে মুক্তি চাই? জানি না।’
‘খোঁজো, খোঁজো।’
‘মেয়েটা জন্মাবার পর খুব আনন্দে ছিলাম ক’দিন। একদিন একটা লোক এল। জেল খাটতে এল আর কী। দিব্যি ভদ্র সুন্দর শিক্ষিত। রেপিস্ট। খুনি। একটা তিন বছরের বাচ্চাকে রেপ করে মেরে ফেলেছে। একটা তিন বছরের বাচ্চাকে! রেপ! ভাবতে পারো? তারপর গলা টিপে মেরেছে। আরে, ওই বাচ্চা তো ওর চাপেই মরে গিয়েছিল। ওর আবার গলা, তাও টিপে মারা। এরা মানুষ? কোনও মানুষ এ কাজ করতে পারে?’
‘মানুষই পারে।’
‘মানুষ হিংস্রতম।’
‘কোনও কোনও শ্বাপদ নিজের ছানাদের খেয়ে ফেলে। কিন্তু শিশুদের যৌননির্যাতন করতে শেখেনি এখনও।’
‘তা বটে।’
‘এই বীভৎস অমানুষতার কাহিনি আমি অন্তত হাজারখানেক জানি।’
‘ঠিক। ঠিক বলেছ। জেলখানায় এসে বুঝেছি ধর্ষণ কত বিচিত্র, ভীষণ, কদর্য ও নির্মম হতে পারে। মানুষের উগ্র কামনা এমনই নিঠুর, তার সঙ্গে জ্যান্ত কচি বাচ্চার কাঁচা মাংস ছিঁড়ে খাওয়ার কোনও পার্থক্য নেই। এখানে শিক্ষিত-অশিক্ষিত ভেদ নেই, ভদ্র-অভদ্র বলে কিছু নেই, পিতা-কন্যা নেই, বয়সের বিচার নেই। বেঁচে থাকা যেন এক মস্ত চোদনাগার।’
‘বেঁচে থাকা আলোকিত ভালোবাসাও কি নয়?’
‘সেই লোকটা, আমার দেখা প্রথম ধর্ষক, খুব জানতে ইচ্ছে করত, কীভাবে ওই কাজ ও করতে পারল। জেলখানায়, বুঝলে, চোর ডাকাত খুনি দাঙ্গাবাজ সব্বাই একাকার, কিন্তু ধর্ষককে কেউ সহ্য করে না। নির্যাতন ও গণপ্রহারে সে জর্জরিত হয়ে যায়। অথচ যারা রেপিস্টকে ঘেন্না করে, তাদের মধ্যেও থাকতে পারে ধর্ষক, জেলে সহবাসী বন্দিদের মধ্যে যৌনবুভুক্ষু পশ্চাদ্দেশ ধর্ষণ জেলের সর্বজনবিদিত ঘটনা। এমনকী, কোনও কোনও জেলকর্মীও গোপনে কাম চরিতার্থ করে। মেয়েদের কারাকক্ষ থেকে বেছে নেয় কামনার শরীর, অথবা কোন সুদর্শন তরুণ বা কোমল কিশোর।’
‘নরকের মধ্যে নরক। নরকের মধ্যে স্বর্গ।’
‘কিন্তু বাইরে থেকে কোনও ধর্ষকের প্রবেশমাত্র মেয়েদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি, নৈতিক আদর্শ ইত্যাদির বিস্ফোরণ ঘটে যায়। ভণ্ডামোয় জগৎ ভরা।’
‘আবার তুমি নিন্দাবাদী হয়ে উঠছ। আবার ডায়োজেনেস?’
‘ডায়োজেনেসের কী দেখলে?’
‘ভণ্ডামোয় জগৎ ভরা, এই দর্শন প্রতিপন্ন করাই লোকটার উদ্দেশ্য।’
‘তুমি কি তা মনে করো না?’
‘আমার মনে করায় কী যায় আসে?’
‘এখানে তুমি বলো, আমি শুনি। আমি বলি, তুমি শোনো।’
‘মনের গতি যে কত বিচিত্র তা মনও জানে না। ধর্ষকের প্রতি ঘৃণার বিস্ফোরণের কারণ মূলত ধর্ষণ বিষয়টির প্রতি ঘৃণা। যদি কেউ এই জঘন্য অপরাধ করেও ধরা না পড়ে, তার নিজের প্রতি ঘৃণা ও অপরাধবোধ থাকতে পারে, সেই বোধের একরকম ভার আছে। নিজের কাছে নিজের সম্মান হারানোর ভার বহন সহজ নয়। তার থেকে রেহাই পেতে সে এই আচরণ করে, বাইরে বোঝাতে চায় সে ধর্ষণকারীকে খুনও করে ফেলতে পারে। নিজেই নিজেকে মিথ্যা নৈতিকতার চাদরে ঢেকে দেয়।’
‘সে তো ভণ্ডামি হল।’
‘না। ঠিক ভণ্ডামো নয়। নৈতিক প্রকাশের মধ্যে দিয়ে সে নিজেকে খানিক শোধন করে নিতে চাইল হয়তো। তার মনে হতে পারে, এই ন্যায়িক প্রতিবাদ, মানবিক ধর্মের প্রতি আনুগত্যের প্রদর্শন তার পাপ কিছু ধুয়ে দিতে পারে।’
‘হয় এমন? সত্যি?’
‘অথবা হতে পারে, তার ঘরে কেউ এর শিকার, সেই প্রতিশোধ সে এভাবে তুলল। অথবা আরও অন্ধকার, আরও আরও ঘোর তমোময় মানসিকতা এমনও হওয়া সম্ভব, কারো মনে মেয়ে দেখামাত্র সম্ভোগের ইচ্ছা জাগে, পৃথিবীতে অগণিত পুরুষ নারীকে সম্ভোগদাসী ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না যেহেতু, তাদের এমন মনে হতে পারে, শালা তুই ভোগ করে এলি আর আমি পাই না। জিঘাংসা জাগ্রত হয়। প্রহারের মধ্যে দিয়ে সেই হীন কামনা তারা চরিতার্থ করতে চায়।’
‘তুমি যখন এমন বিশ্লেষণ করো, আমার সব সঠিক মনে হয়। তর্কের কোনও সম্ভাবনাই থাকে না।’
‘ধর্ষণ ঘৃণ্য অপরাধ মানে যেকোনও ধর্ষণই ঘৃণ্য। কারান্তরালে তা ঘটে চলে কারণ, নৈতিক বোধ যদি লোপ করে দেওয়া যায়, অপরাধই তখন হয়ে ওঠে স্বাভাবিক ক্রিয়া। নৈতিকতা হল দিদিমা-ঠাকুমার বঁটির মতো। রোজ তরকারি কুটতে কুটতে ধার কমে যায়। নিয়মিত ধার না দিলে বঁটি হয়ে যাবে অচল। তাতে জং ধরবে। আবার ব্যবহার না করে ফেলে রাখলেও মরচে তার পরিণতি।’
‘বঁটি নৈতিকতা আর তরকারি কোটা রোজকার চিন্তাদীন কর্মাভ্যাস। এই বোঝাতে চাইছ তো? প্রতীকায়ন। কোনও বঁটিওয়ালি শুনলে ওই বঁটি নিয়েই তোমায় তেড়ে আসবে।’
‘এই খুপরিতে আমায় আর কে পায়, তুমি ছাড়া? বলো, তোমার প্রথম ধর্ষক দর্শনের কথা বলো। বলো তোমার মুক্তির ভাবনা। তুমি এত ভালো শ্রোতা যে আমি তোমার কথা থামিয়ে নিজেই অনর্গল বলতে থাকি। বলো।’
‘তুমি কথা বললে ভালো লাগে। সত্যি বলব? অন্য কারো সঙ্গেই আমার কথা বলতে ইচ্ছে করে না। শুধু মেয়ে আর তুমি।’
‘তোমার কন্যা তোমার অন্তরে ভালোবাসার ধ্রুব স্পন্দন।’
‘সে আমার প্রাণ। আমার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা জীবনের শক্তি।’
‘আমি যদি বোকার মতো, আবেগতাড়িত হঠকারিতা না করতাম, হয়তো তোমার মতো আমারও ফুটফুটে এক মেয়ে থাকত।’
‘থাকত বই কী।’
‘বলো, বলো কী বলছিলে? তোমার ডিউটি অফ করার সময় হয়ে এল। বলতে থাকো।’
‘না না। এখনও আছি কিছুক্ষণ।’
‘ওঃ, এই ঘরে সারাক্ষণই সন্ধ্যা। কিংবা আমার চোখে পরদা পড়ে গেছে।’
‘ডাক্তারি পরীক্ষা করিয়ে নাও। বলো তো আমি রিপোর্ট করতে পারি।’
‘আরে না। মুক্তির পর একেবারে ওর কাছে গিয়ে ডাক্তার দেখাব। এখানে আমি বাতিল, তা কি জানো না তুমি? জীবননাট্য দেখার সুযোগ কেড়ে নিচ্ছে জীবন। সে যাক। তোমাকে পেয়ে আমি ঘ্যানঘেনে বালকের পর্যায়ে নেমে আসি। বলো তোমার বাকি কথা।’
‘সেই প্রথম দেখা ধর্ষক, তাকে রাখা হল ১২-র ঘরে। একেবারে মার্কামারা এগারোজনের সঙ্গে। সবাই জানে মার খেয়ে মরবে, শুধু সময়ের অপেক্ষা। দু-দিন শান্তিতে কেটে গেল। তৃতীয় রাতে ১২-র সর্দার বলল, এই যে, ভদ্রলোক, ইদিকে আয় দিকি। আমার গা-হাত-পা টিপে দে তো একটু। ম্যাজম্যাজ করছে। লোকটা তেরিয়া হয়ে বলল, আমি কি কারো বাপের চাকর? এরপর কী হতে পারে তুমি জানো।’
‘অনুমান করি।’
‘মুখ বেঁধে রামধোলাই। তারপর গুনে গুনে হাট্টাকাট্টা ৬ জন, মতান্তরে ৮, লোকটার পশ্চাদ্দেশ ফুঁড়ে দিতে লাগল। মনে পড়ে ওই বাচ্চাটার কেমন লেগেছিল? মনে পড়ে? মালুম হচ্ছে এখন? এইসব সময় আমরা প্রহরীরা চোখ-কান বন্ধ করে ফেলি তুমি তো জানোই। আধমরা দশায় গেল হাসপাতালে, সেখান থেকে যখন ফিরল, একেবারে ভাঙাচোরা, কুঁজো, খুঁড়িয়ে চলা একটা লোক। তাগড়া জোয়ান থেকে কোলকুঁজো আধবুড়ো।’
‘আহাহাহা।’
‘কেউ কেউ বলল, শাব্বাশ, যেমন কুকুর তেমন মুগুর। বুঝুক কত কষ্ট পেয়েছিল বাচ্চাটা।’
‘বুঝুক, বুঝুক।’
‘আমি ভাবতে লাগলাম, লোকটার পশ্চাদ্দেশ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলেও ও কখনো বুঝবে না একটা তিন বছরের বাচ্চার যন্ত্রণা কতখানি ছিল, কেমন ছিল। কারো পক্ষে তার তুলনীয় শাস্তি খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। অত্যাচারের বিনিময়ে অত্যাচার হল, এই যা। ওকে ওই সেলে আর পাঠানো হল না। গেল মোটের ওপর শান্ত ৫-এর ঘরে।’
‘তারপর?’
দক্ষিণের দেওয়াল একটানা বলে যায়, ‘শিক্ষিত লোক। ধর্ষক ও খুনি হলেও তাকে ভদ্রলোক বলা হয়। জেলে সে বুঝেছে, সমাজে সহানুভূতির বোধ অত্যন্ত শ্রেণিসচেতন। তাকে মন থেকে ঘষে তুলে ফেলা জন্মদাগ তোলার মতোই। শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত সেই লোক জঘন্য অপরাধী হলেও জেলের আধিকারিক ও অন্যান্য কর্মীর চোখে লোকটা ভদ্রলোকই থেকে গেল। ভালো ব্যবহারের বিনিময়ে সে জেলের মধ্যে নির্দিষ্ট সময় চলেফিরে বেড়াবার অনুমতি পেল। ইনার প্যারোল। আপিসে কিছু কিছু কাজও সে করে দেয়, যেমন করেছ তুমি বন্ধু, এই বন্দিত্ব অনেক শিথিল ছিল না তোমার?’
‘ছিল।’
‘অনেকদিন। তা-ই না?’
‘এতকাল পর সেই সময়টুকু ক্ষণস্থায়ী বোধ হয়।’
‘দুঃখ হয় বন্ধু, সেই সময়কার তুমি, সেই যুবকের জন্য দুঃখ হয়। সে তার প্রেমিকার বাবাকে খুন করার অপরাধ সত্ত্বেও একজন উচ্চশিক্ষিত সুদর্শন যুবক, একনিষ্ঠ দেশহিতব্রতী রাষ্ট্রীয় দায়িত্ববান, এক হৃদয়বান প্রেমিক হিসেবেই সে কারাগারে ছিল সমাদৃত ও খুব দ্রুত জেলখানার পরিসরে চলাফেরার অধিকারও সে লাভ করে, যতদিন না, যতদিন না…’
প্রহরী আত্মসংবরণ করে ও প্রসঙ্গে ফিরে আসে। সে বলে চলে, ‘একদিন একজন অপরাধ মনস্তত্ত্বের গবেষক সেই শিশুঘাতী কয়েদিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে এল।’
দক্ষিণের দেওয়াল তার প্রহরায় ছিল। সে একেবারে অভিব্যক্তিহীনভাবে সেই প্রশ্নোত্তর পর্বের সাক্ষী। সে তার বর্ণনা দিতে লাগল।
গবেষক বলে, আপনার বিচার চলাকালীন আমি আদালতে যেতাম।
ও।
আপনি কি আগে কাউকে যৌননির্যাতন করেছেন?
করেছি।
যোনিভেদী ধর্ষণ? নাকি স্তনপীড়ন বা অন্য কিছু?
যখন যেমন সুযোগ পেয়েছি।
কীরকম?
আমার বাড়িতে রান্না করতে আসত এক মাসি। তাকে রেপ করেছিলাম।
তখন আপনার বয়স কত? ওই মাসির বয়স? যদি জানা থাকে।
কলেজে পড়তাম। ধরুন কুড়ি-একুশ। মাসি, ঠিক জানি না, মধ্যবয়সি।
ধরা পড়েননি, বা আপনার বিরুদ্ধে তিনি থানায় অভিযোগ করেননি?
একটা রফায় এসেছিলাম। তাকে টাকা দিতে হত।
এ ছাড়া? আর ক’জন?
বাসে-ট্রামে সুযোগ নিয়েছি। যতখানি নেওয়া যায়। বুঝতেই পারেন।
বোঝা নিয়ে আমার কাজ নয়। তথ্য নিয়ে কাজ।
বড়ো বুক দেখলেই হাত, ইয়ে, পেছনে ঠেকিয়ে ভিড়ের মধ্যে, ইয়ে…
এই তিন বছরের বাচ্চা মেয়ে, এ তো আপনার প্রতিবেশীর কন্যা, তা-ই না?
হ্যাঁ।
চেনাজানা হয়ে গিয়েছিল?
হ্যাঁ। গদনকে নিয়ে রোজ বিকেলে বেড়াতে যেতাম।
গদন? বাচ্চাটা? তাকে কোলে নিয়ে ঘুরতেন?
হ্যাঁ। অবশ্যই?
যৌননির্যাতনের ইচ্ছা হত?
হ্যাঁ। আঙুল, মানে ওই হিসির জায়গায়, যখন বলত, লাগে লাগে, ব্যথা, ছেড়ে দিয়েছি।
কতদিন এমন করেছেন?
দু-তিন মাস হবে।
কখনো মনে হয়েছে, অপরাধ করছেন?
অপরাধ? না, ঠিক অপরাধবোধ না, ভয় হত, যদি ধরা পড়ে যাই।
ধর্ষণের কথা কি হঠাৎ মাথায় আসে, নাকি পরিকল্পিত?
না। পরিকল্পনা কিছু ছিল না। কোলে ঘুমিয়ে পড়েছিল। আমি ইয়ে, মানে আঙুল দিচ্ছিলাম, হিসি করে ফেলল। ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। ভিজে প্যান্টি খুলে ধুয়ে মেলে দিলাম।
বাচ্চারা প্যান্টি পরে না। ইজের পরে।
ইজের, হ্যাঁ, মানে আমি তফাত জানতাম না।
গদন তখনও ঘুমোচ্ছিল?
হ্যাঁ। সর্দিকাশি হয়েছিল। কাশির ওষুধ খেয়ে একটু বেশিই ঘুমোচ্ছিল।
আচ্ছা। তারপর? কীভাবে আপনার মধ্যে যৌন ইচ্ছা জাগে?
ঠিক মনে নেই। ওর ওই হিসির জায়গাটা, ওটা দেখতে দেখতে উত্তেজিত হয়ে গেলাম। আর কিছু মনে নেই।
আপনি কি সচেতন ছিলেন যে একটি শিশুকে ধর্ষণ করছেন?
হ্যাঁ। কিন্তু নিজেকে আটকাতে পারিনি।
কয়েদির বন্ধু দক্ষিণের দেওয়াল বলে চলে, ‘আলাপচারিতা শুনতে শুনতে মনে হল, এ কোন ভয়ংকর মানুষদের মাঝে আমি মেয়েকে নিয়ে এসেছি! এই জঘন্য পৃথিবীতে কেন আমি সন্তানের জন্ম দিলাম?’
‘পৃথিবী কখনো আজকের চেয়ে বেশি নিরাপদ ছিল না।’
‘অপ্রতিরোধ্য ত্রাস, ঘৃণা, কষ্ট, আরও কত কী আমাকে পাকে পাকে শক্ত করে বেঁধে ফেলল। আমার ভিতর থেকে গলগল করে বেরিয়ে গেল আনন্দ। আমার মেয়েকে পাবার নির্মল আনন্দ। শরীর থেকে সব রক্ত বের করে ফেললে যেমন ফ্যাকাশে হলুদ হয়ে যায় মানুষ, সেইরকম আমার চিত্ত। কিছুতেই ভুলতে পারি না যৌনসন্ত্রাস ও লালসার পৃথিবীতে আমার মেয়েকে নিরাপদ থাকতে হবে। আমি, এক জেলখানার কর্তব্যরত প্রহরী, তাকে কোন নিরাপত্তা দিতে পারি?’
‘বন্দি হে, তুমিও এই জেলখানায় বন্দি।’
‘নিরন্তর ত্রাস ও উদবেগ, ভয় ও কল্পিত যন্ত্রণার মধ্যে আমি সত্যি বন্দি হয়ে আছি। আর কত বন্দি হব ভগবান?’
‘বহুরকম গুমখানা। বহুরকম কয়েদখানা। কতক বাইরে, কতক ভিতরে।’
‘এর থেকে মুক্তি কোথায়?’
‘তোমার কিছুই চাওয়ার নেই দক্ষিণ, তবু কত চাওয়া। মানুষের এই তো পরিণতি।’
‘বন্ধু, তুমি অন্তরে ভালোবাসা লালন করো, তোমার জীবনের উদ্দেশ্য তুমি মুক্তি পেলে উত্তরার কাছে ফিরে যাবে।’
‘কী জানি, মুক্তি পেলে তার কাছে যাব, নাকি তার কাছে গেলে আমার মুক্তি হবে, সঠিক বুঝতে পারি না। ভালোবাসা মানেই কি মুক্তি?’
‘ঠিক, ঠিক বলেছ। ভালোবাসা মানেই মুক্তি। অন্তত কিছুক্ষণের জন্য হলেও মুক্তি। মেয়ে যখন কাছে থাকে, কত কথা বলে, কত ঝগড়া, অভিযোগ, আবদার, কত জ্ঞান তার, কত স্বপ্ন, আমার কিছুক্ষণের জন্য মনে হয় কয়েদখানায় বন্দিদের ফুটিয়ে তোলা হাসনুহানার গন্ধ পাচ্ছি। কোথাও কোনও অপরাধ নেই, ভয় নেই। ভালোবাসার আবেশে আমি কিছুক্ষণের প্যারোল পেয়ে যাই।’
‘তা-ই যদি হয়, কারাবাসী হয়েও যদি আমি অন্তরে ভালোবাসি, তাহলে কি আমি মুক্ত নই বন্ধু?’
‘মনে মুক্ত। দেহে বন্দি। আর দেহ যেহেতু মনের মন্দির, সেহেতু মুক্ত পাখনা থাকতেও তার পায়ে শেকল পরানো।’
‘তাই তো, তাই তো আমি এখন সশরীরে বেরুতে চাই।’
‘আচ্ছা, বেরিয়ে প্রথমেই কি তুমি যাবে নরসুন্দরের কাছে?’
‘কেন জিজ্ঞেস করছ?’
‘তোমার চুল কাটা হয় না কতদিন। চুলে জট পড়েছে। নখ বড়ো হয়ে বেঁকে গেছে, ময়লায় হলুদ। এখানকার নাপিত আর তোমার নখ কাটতে চায় না। তোমার চুলে কালো উকুন, গায়ে সাদা উকুন। স্নান করো না নিয়মিত। তোমার দেহত্বক ক্ষতয় ভরে উঠেছে। দগদগে ঘায়ে মাছি ভনভন করে। সত্যি বলতে কী, তোমার অঙ্গে অত্যন্ত দুর্বাস, কারণ বেশ কিছু বছর হল তুমি দাঁত মাজা ছেড়ে দিয়েছ। শৌচের পর তুমি নাকি জল ব্যবহার করো না, অনেকে বলে। এই জেলখানায় তুমি পাগল বলেও পরিচিত। তোমার কি উচিত নয়, প্রেয়সীর কাছে যাবার আগে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া?’
‘না।’
‘না?’
‘না বন্ধু। আমার ওর কাছে লুকোবার কিছু নেই। পরিষ্কার ঝকঝকে হয়ে ঈশ্বরের নিকটতম অবতার সেজে আমি যাব না। আমি যা, তা-ই। যেমন, তেমন।’
‘যদি তোমার দুর্বাস, ময়লা, দগদগে রস চোঁয়ানো ঘা তাঁকে বিরূপ করে?’
‘কই, তুমি তো আমার প্রতি বিরক্ত নও। তুমি তো ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নাওনি।’
‘আমি যে তোমার অন্তর দেখতে পাই।’
‘কী দেখো তার মধ্যে?’
‘ভালোবাসায় দ্রব, সুন্দর, ভালোবাসায় সুন্দর। দেখতে দেখতে আমিও তোমায় ভালোবাসি। কয়েদিকে ভালোবেসে ফেলা নিষেধ সত্ত্বেও।’
‘সে-ও আমায় ভালোবাসে। কতখানি ভালোবাসে তুমি জানো না।’
‘আমাকে বলো, কতখানি সেই প্রেম?’
‘ওর বাবাকে হত্যা করলাম, রক্ত-মাখা শরীর আমার, বললাম, এই আমি, তোমার পিতার হন্তারক।’
কয়েদি বলে চলল।
দেখো, যা করেছি, তোমার জন্য। যা করেছি প্রেমের জন্য।
হ্যাঁ হ্যাঁ, তা-ই।
এই মুহূর্তে আমাকে ভালোবাসো তো?
হ্যাঁ হ্যাঁ বাসি।
চিরকাল এভাবেই ভালোবাসবে?
হ্যাঁ হ্যাঁ, বাসব।
অপেক্ষা করবে তো?
হ্যাঁ হ্যাঁ করব।
কোন এক অতল বিশ্বাসের ঘোর থেকে কয়েদি বলে চলল, ‘পিতার মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে, পিতার রক্ত মাখা ঘাতককে সে বলেছে, ভালোবাসি। অপেক্ষা করব। এভাবে কেউ কাউকে আগে ভালোবাসেনি। আমি তাকে, সে আমাকে।’
‘বেশ।’
‘কারাগার থেকে বেরিয়ে আমি প্রথমেই চলে যাব ওর কাছে। ভালোবাসা। হ্যাহ, বুঝলে, ওই একটাই শক্তি আমাকে জীবিত রেখেছে। লোহার শেকলে ঘষে ঘষে আমার পায়ের চামড়া ঘেয়ো, খসখসে, চটচটে। গন্ধ। আমি তাকে দুর্বাস বলতে পারি না।’
‘পারো না? দুর্বাসকে যদি সৌরভ বলো, তাহলে সত্যের অপলাপ হয় না কি?’
‘তুমি যা রচিবে তাহাই সত্য। তুমি যা চাহিবে তাহাই সত্য। আমার দেহে কোনও দুর্গন্ধ নেই।’
‘কেন নেই?’
‘আমারই ত্বক, যা একদা স্পর্শ করেছিল আমার প্রিয়তমাকে, তার ওপর ভনভনে মাছি এসে বসতে চায়, আমি বলি, অল্প রস পান করে চলে যাও। তিরতির ডানা কাঁপে। কী এক আরাম ছড়িয়ে তারা উড়ে যায়। আমি হাত বুলিয়ে দিই শক্ত খরখরে কুঞ্চিত ত্বকে, যেন পুঁজরক্তক্ষতময় পুষ্করিণীর পাড়ে জমে-ওঠা ছালচামড়ার অসহায় কর্কশ পাহাড়।’
‘আমি ওষুধ আনিয়ে দিয়েছিলাম, লাগাওনি?’
‘হ্যাঁ হ্যাঁ। তুমি দিলে, আমি লাগাব না? সেইসব অব্যর্থ মলম দিয়ে আমি নম্রভাবে বলি, সেরে ওঠো। তার কাছে যেতে হবে একদিন।’
প্রহরী দক্ষিণের দেওয়াল খানিক চুপ করে রইল। তার মনে আছে, মেয়ের সেদিন এক বড়ো পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। খবর পেল। আনন্দে-উচ্ছ্বাসে অন্য কয়েকজন সহকর্মীকে মিষ্টি খাওয়াতে গিয়ে বন্দিকেও দিল। তখনও এত সখ্য হয়নি। বন্দি বলল, ‘সারাদিন এখানেই কেটে গেল, ঘরে ফেরার পথে বিরিয়ানি নিতে ভুলো না। এখনকার মেয়ে, নিশ্চয় চকোলেট ভালোবাসে, নিয়ো।’
বাড়ি ফিরে বলল, ‘হ্যাঁ রে, খবর পেলাম পাশ করেছিস। কিন্তু কেমন পাশ হলি? কতয় কত পেলি?’
মেয়ে রাগ করে বলল, ‘যাও, আমি ফেল করেছি।’ খুব সুন্দর চোখ মেয়ের। বড়ো, টানা, বাঙময়। সেখানে টলটল করছে অভিমানী অশ্রু। ‘কক্ষনো তুমি থাকো না। আমার জন্মদিনে না, স্কুলের ফেস্টে না, কোনও সিনেমায় যাবার সময় না, রেস্তরাঁয় না। শুধু কাজ কাজ আর কাজ। কী কাজ? জঘন্য অপরাধীদের পাহারা দাও। ওদের বাঁচিয়ে রেখে লাভ কী।’
‘ওরকম বলতে নেই।’
‘বলব, বলব, একশোবার বলব। সব্বাই বলে। ওদের মেরে ফেলে না কেন? দেশের টাকা বাঁচে তো। জনগণ কেন মাথার ঘাম পায়ে ফেলা রোজগার থেকে ট্যাক্স দেবে, আর সেই টাকায় অপরাধী পোষা হবে? কেন?’
‘অপরাধীরাও জনগণ। তাদের পরিবার, বন্ধু, আত্মীয় সকলেই জনগণ।’
‘না। তারা সমাজের জঞ্জাল।’
‘অপরাধী মাত্রই জঞ্জাল নয়। আজ এই প্রসঙ্গ থাক মা।’
‘কেন থাকবে? যদি সব অপরাধীকে মেরে ফেলা হত, তাহলে পৃথিবীতে আর কোনও শয়তান থাকতই না। কোনও জেলখানা থাকত না কোথাও। তোমাকেও পাহারা দিতে হত না। তুমি আমার আনন্দের দিনগুলোয় থাকতে আমার সঙ্গে, বাবা। কষ্ট হয় তোমার জন্য। তুমি আর বন্দিরা। সারাদিন। রোজ রোজ। জেলখানার দেওয়াল না বলে আমি তোমায় কয়েদিও বলতে পারি না বাবা?’…
সরল মনে সত্য সরলভাবে প্রতিভাত হয়। একটা বন্দিশালায় সব শালাই বন্দি। ওই আকাশ-ছোঁয়া পাঁচিলগুলো কী সাংঘাতিক নিথর। দুর্ভেদ্য। কিন্তু ওরাও বন্দি। আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাবার উপায় নেই।
কথাগুলি সে কয়েদি বন্ধুকে বলল। কয়েদি একমত। বলল,’হ্যাঁ, ওরা নিথর। বোবা। দৃষ্টিহীন। কিন্তু ভীষণ শক্তিমান। শুধু কান নিয়ে প্রভুর আদেশ পালন করে যায়। ওরা যদি চলতে পারত, কী ভয়ংকর, হেঁটে যাচ্ছে দুর্দমনীয় কান।’
‘কান?’
‘নিশ্চয়। বিশ্বে সবচেয়ে শক্তিমান হল কান। কানের মাধ্যমে, কান দ্বারা, কানের নির্দেশনায় নির্ধারিত হয়ে যায়, তুমি যোগ্য, না অযোগ্য। তুমি প্রতিভা, নাকি থান ইট। তুমি অনুগত, নাকি বিশ্বাসঘাতক।’
‘মাথায় ওদের কান-প্যাঁচানো বৈদ্যুতিক তারের ঝুড়ি।’
‘কাঁটাতার নয়? আমি যখন প্রথম এসেছিলাম, গোল করে প্যাঁচানো কাঁটাতার ছিল।’
‘দুইই আছে। কিছুতেই যাতে ওদের টপকে যেতে না পারো, তার জন্য, দরকার হলে ওরা লোহায় তৈরি ব্রজবিদ্যুতের মুকুট নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।’
‘কী যেন পড়ে তোমার মেয়ে?’
‘ভুলে গেছ? এই সেদিন তোমাকে তার চাকরির সংবাদ দিলাম।’
‘দিয়েছিলে? আচ্ছা? চাকরি?’
‘নগরের পুরভবনে। কম্পিউটার নিয়ে কাজ।’
‘বাঃ, ক্যালকুলেটার এসে যোগ-বিয়োগ গুণ-ভাগে খুব সুবিধে হয়েছিল, আমার মনে আছে। আমিও কিনেছিলাম। দরকার হত না খুব একটা। হিসেবের সময় কোথায়? টাকা পেয়েছি তুলোর মতো। গোনাগুনতির কথা ভাবতেও হয়নি।’
‘ক্যালকুলেটার না, কম্পিউটার।’
‘ওঃ, দুটো আলাদা জিনিস। আমি কক্ষনো কম্পিউটারের পক্ষে ছিলাম না। বিপুল জনসংখ্যার দেশে শ্রমনিবিড় কাজ দরকার। যত বেশি মানুষকে কাজে লাগানো যায়।’
‘সেটা ঠিক। আবার ভুল। দেশ নিজের একক অবস্থান নিয়ে অনড়ভাবে টিকে থাকতে পারে না, আমার মেয়ে বলে। বিশ্বের প্রগতি কখনো অস্বীকার করে চলা যায় না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সমস্ত নিষেধ ও প্রতিবাদের ঊর্ধ্বে। তুমি চাও বা না চাও, সে তোমাকে অধিকার করবেই। প্রত্যেকটি দেশ পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। সারা বিশ্ব এখন একটি গ্রাম, এই ভাবনাই অত্যাধুনিক।’
‘গ্রাম কেন বলো তো? সারা বিশ্ব একটি শহর নয় কেন?’
‘তোমার কী মনে হয়?’
‘প্রযুক্তি বিশ্বের মানুষের মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে দিয়েছে, গ্রামে সবাই পরস্পর পরিচিত, বিপদে-সম্পদে সঙ্গী।’
‘গ্রাম ভাবনার মধ্যে শান্তি আছে। জীবন অনেক ধীর। যাপন সাধারণ। কিন্তু গ্রাম কি নিঃশত্রু? ঈর্ষাহীন? স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী?’
‘না। দুরাচার ও নির্যাতন, শোষণ ও প্রতিশোধপরায়ণতা সেখানে অনেক বেশি প্রত্যক্ষ।’
‘বিশ্বগ্রাম কথাটির মধ্যে কোনও প্রতারণা আছে কি না তা নিয়ে কেউ ভাবে না।’
‘যেমন?’
‘ধরো, কোনও ছোট্ট দেশ স্বাতন্ত্র্য ধরে রাখতে চায়, বিশ্বগ্রামের ধারণা তার পক্ষে চোখরাঙানি নয় কি?’
‘চোখরাঙানি?’
‘আমরা যেমন চাই তেমন হও দিকি, নইলে ঘাড় ধরে আমাদের মতো বানিয়ে দেব।’
‘তুমি বলছ বিশ্বগ্রাম একটি বিশ্বকারাগার?’
‘কারাগার নিয়ে কেউ ভাবে না।’
‘মুক্তি নিয়েও ভাবে না কেউ।’
‘ক্যালকুলেটার থেকে কম্পিউটারের যাত্রাপথে কোথাও লোহার শেকলের পরিবর্ত তৈরি হল না। বিশ্ব নাকি একটি গ্রাম। তা ভাবতে আপত্তি নেই। শুধু পাশের বাড়িতে ঢিল মারার মতো দেশে দেশে যুদ্ধ আটকানো যায়নি। দুগ্ধজাত পদার্থের মতো বিকিয়ে চলে মারণাস্ত্র।’
‘জেলখানা আজও নির্যাতনের সেরা জায়গা।’
‘বিচার এখনও প্রহসন। কারণ বিচার তথ্য বোঝে, যুক্তি বোঝে না।’
‘না না। যুক্তিজাল বিস্তার করেই তো উকিলবাবুরা বিচারকের টনক নড়িয়ে দেয়।’
‘সে তো ওই সাক্ষ্য আর তথ্যের ক্রিয়া। আমি বলছি, অপরাধ বলে যা ভাবা হচ্ছে, তার সম্পর্কে আরও বিশ্লেষণী, আরও সংবেদনশীল ও যুক্তিনিষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন। ওই তোমার যারা ধর্ষককে মেরে সুখ পায়, তারা কি জানে না, বহু নিরপরাধ অপরাধের মিথ্যে বোঝা নিয়ে আসে জেলখানায়। সত্য ও মিথ্যার খিচুড়ি থেকে চালের চাল ডালের ডাল আলাদা করতে পারবে বিজ্ঞান?’
‘মেয়ে বলে, বিজ্ঞান সেইসব আবিষ্কারকেই গুরুত্ব দেয়, জনজীবনে যার চাহিদা আছে।’
‘জনজীবনে সত্য ও মিথ্যা একেবারে দুধের দুধ জলের জল করে দিলে খুব সমস্যা। তার চাহিদা থাকবে কেন? তবে সত্যিকার অপরাধী আর চক্রান্ত বা পরিস্থিতির শিকার হওয়া মিছে অপরাধী নির্ণয় হোক, জনজীবনে তার চাহিদা নিশ্চয় থাকা দরকার।’
‘তাও আবার হয় নাকি? অপরাধ কি ভাইরাল জ্বর যে ঘরে ঘরে তার জন্য প্যারাসিটামলের চাহিদা থাকবে? আর চাহিদাই যদি না রইল, বিজ্ঞান সে নিয়ে ভাবতে যাবে কেন?’
‘সেটা প্রযুক্তির গল্প। বিজ্ঞান কখনো চাহিদার দিকে তাকায়নি।’
‘মেয়ে বলে, বিজ্ঞানের লব্ধ জ্ঞান শেষ পর্যন্ত মানুষ নিজের কাজেই লাগিয়ে ফেলে। ঠিকই বলে। মঙ্গলে যান পাঠাল, এখন ভাবা হচ্ছে, যদি ওখানে বসত করা যায়। চাঁদে জমি কিনে রাখা যাচ্ছে। তো ধরো, মঙ্গল কেমন, প্রথমে এই জানা উদ্দেশ্য ছিল, একটু জানা হতেই ঘরবাড়ি হয় কি না দেখছে। তার মানে কী দাঁড়াল, বিজ্ঞান লক্ষ্যে পৌঁছোলে জ্ঞানে নেমে আসে, জ্ঞান অবতরণ করে প্রযুক্তিতে।’
‘তার মানে মানুষ আজও পিঁপড়ের মতোই একটা প্রাণী।’
‘সে কীরকম?’
‘দেখোনি, ঝড় বৃষ্টি ভূমিকম্প যা-ই আসুক, ওদের জ্ঞানের নাড়ি টনটন করে ওঠে। ওদের খাদ্য আর ডিম বিপন্ন বোধ করলেই কাতারে কাতারে সেগুলি বহন করে নিয়ে যায় কোনও নিরাপদ জায়গায়। এমনকী আমার বালিশের তলায় পর্যন্ত। খাদ্য ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বাঁচিয়ে রাখার আর্তি। এর মধ্যে মানুষ কীসে আলাদা বলতে পারো?’
‘একরকম হলেই বা কী এসে যায়? শেষ পর্যন্ত সবাই তো কেষ্টর জীব।’
‘এই তো ভগবানের লাইনে চলে এলে।’
‘না এসে পারা যায়? তিনিই মুক্তি। তিনিই বিপত্তারণ।’
‘এই তো দিব্য মুক্তির পথ পেয়ে গেছ।’
‘তিনি মুক্তির মুক্তি। তিনি মুক্তেশ্বর।’
‘বিপদ তাড়ানো যদি ভগবানের কাজ, তাহলে বিপদ প্রেরণ করেন কে?’
‘আমার মা বলত, ভক্তকে বিপদে ফেলে পরীক্ষা করেন ভগবান। ভক্ত কতখানি অনুগত, কত তার বিশ্বাস, বুঝেশুনে তাকে উদ্ধার করেন।’
‘মা-কে এই সংবাদ কে দিয়েছেন?’
‘জানা হয়নি। বোধহয় আত্মোপলব্ধি।’
‘তা হবে। কিন্তু আমি দেখছি, ঈশ্বরও জননেতার মতো বিশ্বাস, আনুগত্য ও ভক্তির জন্য কাঙাল। এমনকী আচরণেও মিল পাওয়া যাচ্ছে। বিপদে ফেলে বিপদ থেকে উদ্ধার করা, আনুগত্যের অভাব বুঝলে বিপদপঙ্কে ডুবিয়ে মারা, ভক্তি কম পড়লে পায়ে বেড়ি পরিয়ে বন্দিশালায় প্রেরণ, একরকম না?’
‘তুমি তোমার দিক থেকে দেখছ। আমি যে কিছুই না করে, কিছুই না বুঝে বালের জেলখানায় দক্ষিণের দেওয়াল হয়ে রইলাম, সেইবেলা?’
‘তুমি কী হতে চেয়েছিলে? মেয়েদের গণশৌচালয়ের দেওয়াল?’
‘আমি দেওয়াল হতেই চাইনি। শুনছ? এই প্রহরা, এই বিশাল পাঁচিলের জঙ্গল, এই বিড়িখেকো সহমর্মিতা, পাতাখোর বন্ধুত্ব, ছিলিমের ধোঁয়ার মতো নিরুৎসাহী দিন, কুৎসিত জঘন্য অপরাধীদের নিশ্বাস গায়ে মাখার নারকীয় জীবন আমি চাইনি। আমি বন্দি হয়ে গেছি। আমার মেয়ে ঠিক বলে। বন্দি। আমি বন্দি। আমি বন্দি।’
‘শান্ত হও দক্ষিণ, আমার মা বলত, তোমার যখন কোনও কষ্ট হবে, কোনও অভাব বোধ হবে, তুমি আরও বেশি কষ্ট পাওয়া মানুষের কথা ভাববে, আরও বেশি অভাবগ্রস্তের দিকে তাকাবে। তখন তুমি নিজেকে সুখী ভাববে। তোমার কোনও অভাববোধ থাকবে না।’
‘তোমার মা একজন বিদুষী নারী।’
‘সন্দেহ নেই। তিনি ছিলেন মেয়েদের কলেজের অধ্যাপিকা। কিন্তু ওই কথাগুলো তুমি মেনে নিলে নাকি?’
‘হ্যাঁ। গভীর সব কথা। মানতে ক্ষতি কী। তুমি অবশ্য বলেছ, বিনা তর্কে কোনও উপদেশ মেনে নেওয়া মূর্খামি। অথচ ছোটোবেলা থেকে আমরা বিনা প্রশ্নে বড়ো হয়েছিলাম। প্রশ্ন করা ছিল অবিনয়, নিন্দনীয়। এখন তোমার মায়ের উপদেশ বিষয়ে তর্ক তুলে লাভ নেই, কারণ আমার সামনে শুধু তুমি, একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক অথচ যে এক জঘন্য নিকৃষ্ট হত্যাকারী হিসেবে সাজাপ্রাপ্ত।’
‘আর?’
‘যার বন্দিত্ব আমার চেয়ে দীর্ঘ ও কষ্টকর।’
‘আর?’
‘যে আমার চেয়েও অনড়।’
‘তারপর?’
‘আমার কারাবাসের মেয়াদ আমার চাকরি, তার কারাবাস অনিঃশেষ।’
‘না না না। আমার কারাবাস শীঘ্র শেষ হবে। মুক্তি চাই। আমি মুক্তি চাই।’
‘আমিও চাই। তোমার সঙ্গে কথা বললে বুঝতে পারি বহু বন্ধন থেকে বহুতর মুক্তি কাম্য। প্রথমে কোন মুক্তি চাইব জানি না।’
‘আর যে তোমার সামনে আছে?’
‘সে আছে মুক্তির প্রতীক্ষায়। একমাত্র মুক্তি, এই সংশোধনাগারের বাইরে বেরুনো।’
‘দুই, তার কাছে যাওয়া।’
‘মাত্র দুই।’
‘তুমি বিচলিত?’
‘কীসের বিচলন?’
‘আমি তোমার চেয়ে অধিকতর বন্দিত্ব ও দুর্দশায় নেই?’
‘তোমার তুলনায় আমার বিচলিত হওয়ার কোনও কারণ আমি নিজেই খুঁজে পাই না।’
‘এ বিষয়ে ঢের তর্ক হতে পারে। সেই তর্ক আমি করব। আজ আমার অনর্গল অবিরাম কথা বলতে ভালো লাগছে। তোমার খারাপ লাগছে না তো?’
‘প্রথমত খারাপ লাগছে না। দ্বিতীয়ত, যদি লাগত, তবু আমি তোমার সঙ্গে কথা চালিয়ে যেতাম, কারণ বন্ধুর ভালো লাগার জন্য এটুকু আমাকে করতেই হত। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা।’
‘যা-ই ভাবো, নিচু গলায় ভাবো।’
‘কেন? ভয় কাকে? কীসের ভয়?’
‘আমার আর ভয় কীসের? ছাড়া পেলেই আমি তার কাছে চলে যাব। আমি তোমার জন্য বলি। বন্দির সঙ্গে প্রহরীর বন্ধুত্ব অনেকের অশালীন মনে হতে পারে।’
‘তুমি কি ভাবো, এসব চাপা আছে? কারাগারের কান কত লম্বা তুমি জানো না?’
‘তা অবশ্য।’
‘তুমি মনে মনে কথা বললেও ওরা শুনতে পায়। এই যে রোজ চে লিখছ, সেই নিয়ে এখন বিস্তর হাসাহাসি।’
‘কীসের হাসি?’
‘বলে পাগল। দেওয়ালে কেউ চে লেখে নাকি এখন? লিখতে হয় ব্যাবসা সত্য জগৎ মিথ্যা। লিখতে হয় তালিবান।’
‘এরা কি চে-র চেয়েও চে-তর?’
‘তার আমি কী জানি? ওরা বলে। আমি শুনি।’
‘বেশ করো। আমার চে গভীর হচ্ছে। আমার মুক্তিমান চে। ওদের কথা ছাড়ো। কত আসে, কত যায়। চিরস্থায়ী নাম মিকেলেঞ্জেলো। স্পার্টাকাস। প্লেটো। অয়লার কিংবা ধরো গ্যালিলিও, ব্যোদলেয়র।’
‘ওসব লেয়ার-টেয়ার ছাড়ো। কী একটা বলছিলে, তা বলো। আমি চে বুঝি না, লেয়ারেও আমার ব্যুৎপত্তি নেই।’
‘একটা বিড়ি ধরাবে? দু-টান দিয়ো। বলছিলাম…’
‘ঠিক দু-টান কিন্তু। তোমার খুপরিতে জ্বলন্ত বিড়ি ঢুকেছে জানলে চাকরি যাবে।’
বন্ধু দেওয়াল বিড়ি ধরাল। লোহার দরজার তলা দিয়ে সেঁধিয়ে দিল। খানিক পরেই একই পথে ফিরে এল জ্বলন্ত অবশেষ। সে বলল, ‘বলছিলাম, নিজেকে অতখানি বন্দি মনে হচ্ছে যখন, খানিক আমোদ করে নাও। জ্বালা কমবে।’
‘দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোমরের হাড্ডি ক্ষয়ে গেল শালা। এখানে নাকি আমোদ করব।’
‘তোমার হাতে আগ্নেয়াস্ত্র আছে।’
‘তো? ও তো মরা।’
‘শবসাধনা করো। মড়া জাগিয়ে তোলো। শ্মশানের গন্ধের মধ্যে পুনরুজ্জীবনের গন্ধ লুকিয়ে থাকে, থাকে বিদ্রোহ পোড়ার গন্ধ। ঘৃণা পুড়তে থাকার সৌগন্ধ। পোড়া প্রেমের সৌরভ। তুমিও তোমার বন্দুক বাজাও। বন্দিত্ব একপ্রকার মৃত্যু। আর বন্দুক বিশল্যকরণী।’
‘ধুসস।’
‘বাজাও বাজাও। বারুদের গন্ধে, শাসানোর শব্দে, আগুনের ঝলক ও উত্তাপে নিজেকে ক্ষমতাবান মনে হবে। ক্ষমতার স্বাদ পেলে নিজেকে আর বন্দি মনে হয় না কিছুক্ষণের জন্য হলেও। আমার পদযুগলে আর শেকলে কেমন ক্ষমতা ও অক্ষমতার গলাগলি, বললাম না? চালাও বন্দুক। বন্ধু। গুলি করো। কীরকম চনমনে লাগবে দেখো।’
‘সে তোমার দশা দেখেই বুঝতে পারছি। কিন্তু অকারণে বন্দুক চালালে আমার চাকরি যাবে।’
‘অকারণে কেন? তুমি বলবে আমি পালাবার চেষ্টা করেছিলাম। আত্মরক্ষার জন্য, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার দায়িত্বে, একজন দাগি সমাজবিরোধীর উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিতে তুমি গুলি চালিয়েছ। এভাবেই তো কত বিপ্লবীর মৃত্যু ঘটে। পুলিশ ও অপরাধীর পলায়ন নাট্যানুষ্ঠান, যেখানে পালানো অভিনয়, গুলি অব্যর্থ ও আসল।’
‘ওসব আমার দ্বারা হবে না ভাই।’
‘হবে বন্ধু, হবে। আগুনের অমর্যাদা কোরো না। নাও। শুরু করো।’
‘তুমি পালাবার চেষ্টা করেছ তা কেউ বিশ্বাস করবে না। কোথা দিয়ে পালাবে? কীভাবে?’
‘হুমম তুমি বলবে আমি ওই খাবারদাবার দেওয়ার ফোঁকর গলিয়ে মাথা বের করেছিলাম। শক্ত দাঁতে কামড়ে ধরেছিলাম তোমার কোমরের বেল্ট। ইত্যাদি।’
‘ওই ফোঁকর দিয়ে মাথা গলানো সম্ভব নয়।’
‘কে বলে? দুনিয়ায় এমন কোনও ছিদ্র নেই যেখান দিয়ে মানুষ মাথা গলায় না।’
‘ধুস। মাঝে মাঝে তোমার কথার অর্থ বুঝি না আমি।’
‘দরকার কী? আমিও মাঝে মাঝে নিজের কথা বুঝি না। তাতে কিছু এসে যায় না। তোমার চাকরির জন্য দরকার রাজার আদেশ বুঝতে পারা। আর আমি চাই কথা। যেকোনও কথা। যেমন, তুমি যে বললে, বিজ্ঞান থেকে জ্ঞানে, জ্ঞান থেকে প্রযুক্তিতে অবতরণ, তা, সেটা উত্তরণ নয় কেন? উত্তর দাও।’
‘সত্যি বলব? এসবের উত্তর আমি জানি না। তবে তোমার সঙ্গে থাকতে থাকতে আমার একটা স্বভাব গজিয়েছে।’
‘স্বভাব গজায় নাকি? স্বভাব তো স্ব ভাব, ও নিজের মধ্যেই থাকে। বলো অভ্যাস।’
‘অভ্যাস বেশি চর্চা করলে স্বভাবে পরিণত হয়। মেয়ে বলেছে।’
‘তা, আমার সঙ্গদোষ তোমায় কী স্বভাব দিল?’
‘প্রশ্ন করা। নিজের মধ্যে নিজে ভেঙে ভেঙে দেখা, প্রিজমে সত্যি সূর্যের দেখা মেলে কি না।’
‘সূর্যের সাত রং। আসলে আরও অনেক বেশি রং। আমাদের চোখ ধরতে পারে না।’
‘তা হবে। কিন্তু মেয়ে যখন বুঝিয়ে দেয়, মনে হয়, এর চেয়ে সঠিক আর হতে পারে না। সে যেন অব্যর্থ টিকা। দিলেই রোগ থেকে মুক্তি।’
‘কী বোঝায় মেয়ে?’
‘সে বলে, বিজ্ঞান যতক্ষণ নিজেকে প্রশ্ন করবে ও উত্তর খুঁজতে খুঁজতে এগোবে, ততক্ষণ জ্ঞান বৃদ্ধি হবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে রাখা সোনার মতো, আর সেই সঙ্গে প্রযুক্তির জটিলতম প্রয়োগ মানুষের কাজের পথ সরলতর করে তুলবে। আলাদা করে ভাবলে এই যাত্রাপথে জ্ঞানের বৃদ্ধি ও প্রযুক্তির উন্নতি ঘটে কিন্তু যদি বিজ্ঞান, জ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্রে ফেলে অবস্থান ও গতিপথ বিবেচনা করা যায়, তাহলে যে কেউ বুঝতে পারবে বিজ্ঞান থেমে গেলে জ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি অসম্ভব। তাহলে, বিজ্ঞান একদিকে স্বয়ং সঞ্চরমাণ অন্যদিকে সে দুটি অপেক্ষক সত্তার বিকাশ ঘটায় যারা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাহলে বিজ্ঞান একদিকে আরোহণ করে এবং অন্যদিকে অবরোহণ করে।’
‘এই তিনজনকে কি ট্রেনের ইঞ্জিন ও কামরার মতো সরলরৈখিক সম্পর্কে ফেলা যায় না? যারা সংযুক্ত, নির্ভরশীল, কিন্তু একমুখী?’
‘সে কথা আমিও মেয়েকে বললাম। মেয়ে বলল, সেটা সেই তার কৈশোরে দেখা দুনিয়ার মতো হবে, যখন সে মনে করত সমস্ত অপরাধীকে মেরে ফেললে জগৎ অপরাধমুক্ত হয়ে যায়।’
‘ঠিক বুঝলাম না।’
‘সে তো জানত না, অপরাধবিহীন সমাজ অসম্ভব। সে বুঝত না, যাকে অপরাধী বলা হচ্ছে, সে কোনও কিছুর সাপেক্ষে অপরাধী বিবেচিত হতে পারে, সে নির্দোষ হতে পারে ইত্যাদি। আজ সে জানে নিষ্পাপে পাপ ঢুকিয়ে দেওয়াই অপরাধের কাজ। নিত্যনতুন ভাইরাসের মতো নিত্য মানুষের মধ্যে তৈরি হয় অপরাধের ইচ্ছা। সে জানে, অপরাধীরও আছে জীবনের অধিকার, সেই অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে না।’
‘বটে?’
‘আমার মেয়ে প্রাণদণ্ডের ঘোর বিরোধী। সে বলে, প্রাণদণ্ডের চেয়ে বড়ো বর্বরতা আর নেই। কোনও শর্ত, কোনও বিচার, কোনও উদ্দেশ্য দ্বারা প্রাণদণ্ডের অসভ্যতা সমর্থন করা যায় না।’
‘আর কী বলে?’
‘সে বলে, মানুষের সমাজ গঠনের মধ্যে কোনও মেধার পরিচয় নেই। সবকিছু, সব নিয়ম, সব দৃষ্টিভঙ্গি আবার নতুন করে গড়ে তোলা দরকার। মানুষের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করার যুগ এসে গেছে। যে কেউ তার নিজের সাপেক্ষে কোনও কাজ প্রয়োজনীয় বিবেচনা করে। এই স্বতন্ত্র সত্তার পাশে নিরন্তর একজন বিচারক থাকে বলেই একজন অপরাধী বিবেচিত হয়। বিচারক না থাকলে প্রত্যেক অপরাধী নিজে নিজের কার্যক্রম বিষয়ে গ্রহণযোগ্য যুক্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারত। সমাজের পুরো ব্যবস্থা ও মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের নির্মাণবিধি সম্পূর্ণ অন্যরকম হত।’
‘তা হত। একেবারে নৈরাজ্যবাদী অবস্থানের চূড়ান্ত হয়ে যেত। মেয়েকে বোলো, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ধারণা তখনই সম্ভব যখন ব্যক্তিস্বার্থবাদ অতিক্রম করা যায়। আর তোমার মেয়ের মতে চললে কি বিজ্ঞান জ্ঞান ও প্রযুক্তির রেলগাড়ি গড়ে উঠত?’
‘তা বলতে পারি না। মেয়ে বলেছিল, বিজ্ঞান এখানে দাত্র। তাই গ্রহিত্রর সঙ্গে তার সরলরৈখিক সম্বন্ধ অসম্ভব।’
‘বিজ্ঞান দাতা কেন? দাতা-গ্রহীতার ব্যাখ্যার মধ্যে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর ও জীবনদাতার চিন্তার সাদৃশ্য আছে। সেই চিন্তা একরকম বন্দিত্ব। সে-ও এক শৃঙ্খল। কোনও দাতা ও গ্রহীতা একই সরলরেখায় আসতে পারে, যদি পরস্পরের সম্বন্ধ অন্য দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করা যায়। বিজ্ঞান সার্থক হত না যদি জ্ঞান সঞ্চয় না হত, যদি জ্ঞান আত্মপ্রশ্ন না করত, জ্ঞান অর্থহীন হয়ে যেত যদি না তার প্রয়োগ ঘটানো সম্ভব হত। অর্থাৎ তিনটি বিষয়, পরস্পর নির্ভরশীল। শুধু তা-ই নয়, প্রযুক্তির জটিলতর যাত্রা সরলতর পথের সন্ধানে জ্ঞান উদবুদ্ধ করে, জ্ঞান আত্মানুসন্ধান করে উত্তর না পেলে বিজ্ঞানের মুখাপেক্ষী হয়।’
‘তা-ই হবে।’
‘বেশ, তর্কে অবসান চিহ্ন বসিয়ে দিলে।’
‘তর্কে বহু দূর। তার চেয়ে ভালো লাগে যখন তুমি নিজের কথা বলো। কিংবা আমি বলি আমার কথা।’
‘আমার আজ বড়ো ভালো লাগছে। তার কথা মনে পড়ছে।’
‘এমন একদিনও কি যায় যেদিন তোমার তাঁকে মনে পড়ে না?’
‘না। মনে পড়ে। সারাক্ষণ। ধরো, এই তোমার সঙ্গে কথা বলছি, সমান্তরালভাবে তার কথা ভাবছি। এমনকী, যখন হত্যা করছিলাম, তখনও আমি তাকেই ভাবছিলাম।’
‘ওঃ।’
‘যেন মনের ভিতর মন, চিন্তার ভিতর চিন্তা। সেই ভিতরের চিন্তার ওপর আমার কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। সে স্বরাট। যকৃতের মতো। কিংবা হৃৎপিণ্ডের মতোও বলতে পারো।’
‘কী যে তুমি বলো।’
‘মাঝে মাঝে কী মনে হয় জানো? আমি তো কয়েদি হতে চাইনি, আমার আদর্শ ছিল, লক্ষ্য ছিল, স্বদেশানুগত্য ছিল, মানুষের মঙ্গলের জন্য আমি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলাম। রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো ও তার অভ্যন্তরে পচন, দুরভিসন্ধি ও দুর্বৃত্তি, দুর্নীতি একেবারে নিঃশেষ করে দেবার ব্রত ছিল আমার। তার জন্য সমস্ত আদেশ আমি নিঃশর্তে নির্বিচারে পালন করেছি।’
‘নিশ্চয়। তুমি একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক।’
‘তুমি যখন আনুগত্যের ব্রত গ্রহণ করো, তোমাকে নিজের মনের ভিতরকার বিচার ও জিজ্ঞাসা ভুলে যেতে হবে। আনুগত্য অর্থ তুমি অন্য কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের শুভানুধ্যান বিশ্বাস করো। তোমার লক্ষ্য ও তোমার পরিচালকের লক্ষ্য এক। তোমাকে কেউ কিনতে পারে না, কিন্তু যখন তুমি নিজেকে উৎসর্গ করেছ, তখন তোমাকে প্রতিপালন করার দায়িত্ব সেই কেন্দ্রীয় সত্তার যেখান থেকে তুমি পাও নির্দেশ ও ক্ষমতা। আমার সেই আত্মনিবেদিত জীবনে আমি মুহূর্তের জন্যও বন্দি এমত বোধ করিনি। ওঃ, কী প্রবল ছিল সেইসব দিন।’
‘বলো, বলো। তোমার সেই জীবনের কথা বলো।’
‘কত প্রদীপ্ত লক্ষ্যের প্রতি ধাবমান, হত্যা করেছি ধানের খেতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া পচা বিকল্প রাজনৈতিক ছদ্ম দেশহিতব্রতীদের, হত্যা করেছি বহু বহু দুর্বৃত্ত, দুর্নীতিবাজ, উদ্যত ছিলাম দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে দুরভিসন্ধিধারী নাগরিক চিহ্নিত করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পবিত্র দায়িত্বগ্রহণে।’
‘হ্যাঁ হ্যাঁ। তা-ই তো।’
‘কিন্তু একটা খুন, মাত্র একটা খুন আমার যাবতীয় পবিত্র কর্মের ইতিবৃত্ত হনন করেছে। দেশহিতব্রতে যে হত্যা, তার জন্য আমি অপরাধী গণ্য হইনি। কয়েদ হইনি। ব্যক্তিগত ভালোবাসা নিরাপদ করতে চেয়ে যে হনন, তা আমাকে কয়েদখানায় ঢুকিয়ে দিল। অর্থাৎ, তুমি যখন নিজেকে নিবেদন করেছ, তোমার জীবনে আর ব্যক্তিগত বলে কিছু থাকে না। উৎসর্গীকৃত তুমি, যে কর্মের জন্য আরও আরও বেশি দায়িত্ব ও ক্ষমতা লাভ করছ, আরও নির্ভরযোগ্য ও মহিমান্বিত, সেই একই কর্মানুক্রম যদি তুমি করে ফেলো ব্যক্তিগত জীবনের স্বার্থে, সঙ্গে সঙ্গে তুমি হয়ে যাও অপরাধী।’
‘তা-ই তো দাঁড়াচ্ছে।’
‘ওই লোকটা, আমার প্রেমিকার পিতৃদেব, বিপুল অঙ্কের অনুদান দিত, দলের হয়ে গ্রহণ করে যে নৈর্ব্যক্তিক তহবিল, সবাই তার ওপর নির্ভর। কিন্তু এককভাবে দলের কেউ ওই অনুদান পকেটে পুরলে সে হবে ঘুষখোর। পূর্বেকার সমস্ত মহিমা, মুছে যাবে মুহূর্তে। কেউ তার পাশে থাকবে না তখন। সেই হল নিয়ম।’
‘সে যাক। তোমার কথা বলো।’
‘আমার কোনও অনুশোচনা নেই। অভিযোগ নেই। সেইসব আদর্শবাদ আমার বুকের ভিতর চুপচাপ তালাবন্দি আছে, আমার মায়ের টিনের তোরঙ্গে রাখা লেপ-কম্বলের মতো। সঙ্গে আমার শীতের পোশাক, ছোটোবেলার ছোটো ছোটো পোশাক, যেগুলি নিয়ে মা মাঝে মাঝে গন্ধ শুঁকত ওই রোদ্দুরে দেওয়ার আগে।’
‘আর বলত, দেখ, এর মধ্যে তোর ছোটোবেলার গন্ধ। দুধ-দুধ। মিষ্টি-মিষ্টি।’
‘হ্যাঁ। দুধ-দুধ। মিষ্টি-মিষ্টি। কিন্তু আমি কখনো সেই গন্ধ পাইনি। ন্যাপথলিন আর সারাবছর চাপা এক সোঁদা গন্ধ শুধু।’
‘অতীতের গন্ধও।’
‘এখন, ওই পশ্চিমের শ্মশানে কোনও ভালোমানুষ পুড়তে থাকলে যে গন্ধ আমি পাই, বুঝলে, তার সঙ্গে আমার ওই অব্যহৃত নীতি ও আদর্শের গন্ধে মিল আছে। কিন্তু মায়ের মতো, তোরঙ্গ খুলে আমি বছরে অন্তত একবার তার আঘ্রাণ নিতে চাই না।’
‘তুমি কী চাও?’
‘আমি শুধু তার কথা ভাবি। ভালোবাসার কথা। কত-না ভালোবেসেছি আমি তাকে, সে আমাকে। পৃথিবীতে কেউ কাউকে এমত ভালোবাসে না।’
‘এমন তো নয় যে তুমি আসলে তোমার ভালোবাসাকেই ভালোবাসো? এক লুকোনো দর্পণে তুমি তোমার ভালোবাসার প্রতিবিম্ব যেই দেখলে, অমনি স্থির হয়ে গেলে। তোমার পলক পড়ে না। তুমি নিশ্চল। আস্তে আস্তে তুমি স্বচ্ছ হয়ে যাচ্ছ। কেউ তোমাকে দেখতেও পাচ্ছে না। কিন্তু তুমি আছ, আর তোমার ভালোবাসা।’
‘তোমার মেয়ের নীতিকথামূলক পাঠ্যপুস্তকে পড়েছ বুঝি?’
‘ধরেছ ঠিক। কিন্তু এভাবেই কি মানুষ মুছে যায় না? আদর্শবাদী কত মানুষ? তুমি এক আদর্শ নিয়ে যাদের পবিত্র হত্যা সাধন করেছ তারাও অন্য এক আদর্শের বাহক। তারা মুছে গেছে।’
‘সে যাক গে। ও নিয়ে আর ভাবি না। ওদের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে গলায় মালা দেওয়ার পবিত্র দায়িত্ব ছিল না আমার। আমরা ওদের আদর্শ মুছে ফেলতে চেয়েছি বলেই ওদের হত্যা করেছি। ঠিক যেমন দুরারোগ্য ও সংক্রামক ব্যাধি আক্রান্ত প্রাণী মেরে ফেলতে হয়।’
‘তুমি তোমার হত্যা ও খুন নিয়ে কিছু বলো না সচরাচর। আজ তোমার কথা শুনে আমার মেয়ের সেই পরীক্ষার ফল বেরুবার দিন মনে পড়ছে। হাসিও পাচ্ছে অল্প।’
‘হ্যাঁ, মেয়ে বলেছিল, সব অপরাধীকে ধরে নিকেশ করে দেওয়া হচ্ছে না কেন? তাহলেই জগৎ থেকে অপরাধ নির্মূল হয়ে যাবে। বিশ্ব হবে নির্মল। সরল বালিকার সরল কথা। হাসি তো পাবেই।’
কয়েদি কথা বলল না আর। ভাবতে লাগল। তার ভালোবাসার সেই নারী, যার সঙ্গে এমন কত কথা সে বলত। ভারী ও গভীর অর্থপূর্ণ। অথবা অর্থহীন। অথবা বিদ্রুপাত্মক। কিংবা প্রেমাবেগপূর্ণ। যা-ই হোক-না কেন, শেষ পর্যন্ত তাদের নিষ্পত্তির পথ ছিল ভালোবাসা। সেই ছিল তার দিনশেষের ঝুলিভরা আনন্দের সঞ্চয়।
আজ সে কাছে থাকলে, এই ময়লা ছিন্ন পরিচ্ছদ, বাঁকানো গুটিয়ে ওঠা হলুদ নখর, চিটচিটে জটা-ধরা উকুনের আবাস কুন্তলদাম, দেহের খাঁজে আন্ডাবাচ্ছা নিয়ে জাঁকিয়ে সংসার পেতে-বসা সাদা চাম উৎকুনের দল কিছুতেই পাত্তা পেত না। সর্বাঙ্গে ঘা-চুলকুনি থাকত না এতটুকু। সব কাজের পর, স্নানান্তে, সে ওই বাড়ি গিয়ে বসত এক কাপ চা নিয়ে। প্রিয়তমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়েছে কত, যখন আশপাশে কেউ নেই। সে হাত বুলিয়ে দিত চুলে। কী ঘন আর নরম চুল আপনার, বলত। আরামে কোলই কোলবালিশ করে ঘুমিয়ে পড়েছে কিংবা সম্পূর্ণ জেগে উঠেছে তার যোনিরসপানের ইচ্ছায়। সেই যোনি এক আশ্চর্য মধুকুঞ্জ। একদা এইসব নিয়েই তার দিবসরজনি কেটেছে। হ্যাঁ। নিশ্চয়। প্রেয়সী আজও এই বন্দির অপেক্ষায় আছে।
সে ঘুমিয়ে পড়তে লাগল। দেওয়ালও নির্বাক। ঘেয়ো দুর্গন্ধ, কীট ও মললিপ্ত ঘুমন্ত দেহের ওপর খেলা করে কোঁৎকা ও হোঁৎকা ইঁদুর। তার ভুক্তাবশেষ খেয়ে পুলকিত, পুষ্ট। আরশোলা শুকনো খরখরে ঠোঁটের ওপর বসে শুঁড় নেড়ে ইতিহাস ঘাঁটতে থাকে প্রত্নতাত্ত্বিক চুম্বনের ভাঙাচোরা দু-একটি খোলাম সংগ্রহ প্রত্যাশায়।
ইদানীং তার তেলচিটে মলিন বালিশ ও শিয়রে যত্নে রাখা সত্যিকার বইপত্রের আড়ালে, পুবের দেওয়াল ঘেঁষে বিড়ে পাকিয়ে ঘুমোয় এক বৃদ্ধ দাঁড়াশ। কোনও ছুঁচো বা ইঁদুর স্বেচ্ছায় আত্মবলি দিতে এলে খায়, নয়তো উপোস। কখনো বাইরে যাবার প্রয়োজন হলে তার আঁশটে শীতল শরীর কয়েদির ঘুমন্ত শরীরের ওপর দিয়ে চলে যায়, ফিরে আসে। কয়েদি টের পায়, আবার পায়ও না। সবার সঙ্গেই অলিখিত সমঝোতা। শুধু মাংসকীটদের সে কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি।
উত্তরের দেওয়ালে চাপ চাপ শ্যাওলাটে দাগের ভিতর সে যে প্রেমিকার মুখ দেখে অজস্র, যেন ওই দেওয়াল উত্তরার শরীর জুড়ে সজ্জিত তার প্রেয়সীর অজস্র ফোটোগ্রাফ, কেউ এসে রোজ সেগুলি নতুন করে সাজিয়ে দিয়ে যায় আর কয়েদি গভীর অভিনিবেশে দেখে, সেরকম, দেখতে দেখতে একদিন হঠাৎ অপরিসর মেঝেয় গটগট করে চলেফিরে বেড়ানো ম্যাগট দেখে চিৎকার করে ওঠে। সেই ভীষণ গর্জন শুনে ছুটে এল কারারক্ষীরা বন্দুক তাক করে। ক্রমে সেই মাংসকীটেরা ছেয়ে ফেলতে লাগল বালিশ বিছানা দেওয়াল বই কালো ছোপ ধরে যাওয়া শৌচাগার। তার মনে হচ্ছিল, সে পাগল হয়ে যাবে। এত এত এত কীট তার মাথায় ঢুকে পড়ছে। মনে, বুকে, চিন্তায়। সে গর্জন করছে, মেরে ফেলো। মারো, মারো ওদের। মাংসভুক কীট। কোন সাহসে ওরা উত্তরার শরীরে বাইতে যায়?
কোথায় কীট? কীসের কীট?
অবশেষে চিকিৎসক আবিষ্কার করেন, কয়েদির ঊরু কুরে কুরে খেয়ে ফেলেছে কীট। উকুনের দংশনে, নাকি ইঁদুর কামড়ে দিয়েছিল, ক্ষতমুখে গজিয়ে ওঠা মাংসকীট হৃষ্টপুষ্ট খসে পড়ছে টুপটাপ।
‘এ তো ভীষণ যন্ত্রণা। এভাবে মাংস খেয়ে নালি করে দিয়েছে। সহ্য করলে কী করে?’
‘পারি। আমি পারি। আমাদের ট্রেনিং নিতে হয়। আগে ওদের মারুন। ঘর ছেয়ে গেছে। উত্তরার শরীরে বাইছে।’
‘উত্তরা?’
‘দেওয়াল। উত্তরের দেওয়াল। ওখানেই ছবি দেখতে গিয়ে আমি ওই শয়তানের বাচ্চাগুলোকে দেখে ফেলেছি। উফফ, কত যে। হাজার হাজার। নাকি লক্ষ লক্ষ। আমার মাথায় ঢুকে গেছে, বুকে, হৃৎপিণ্ডে। আমার বই খেয়ে ফেলছে। বালিশ ফুটো করে দিচ্ছে।’
‘অত নয়। দিনের পর দিন তুমি শুয়ে ছিলে নিশ্চয়। ওগুলো তোমার ঊরু কামড়ে ছিল। যেই দণ্ডায়মান হলে, খসে পড়ল কিছু। তুমি এখন হাসপাতালে থাকবে কিছুদিন। তোমার সেল পরিষ্কার করা হবে।’
‘একটাও কীট যেন না থাকে ঘরে।’
‘তুমি যদি গায়ে পুষে না রাখো, ঘরেও থাকবে না। এবার বলো, উত্তরের দেওয়ালে কীসের ছবি?’
‘ছবি। আমি দেখতে পাই। মুখ। শুধু পরিচিত মুখ, অবয়ব, ভঙ্গিমা। পুবের দেওয়ালেও আছে। জ্ঞান। জ্ঞানের ছবি।’
‘নারী দেখো বুঝলাম, অ্যাপোফেনিয়ায় ভুগছ তুমি। ওষুধ খেতে হবে। কিন্তু জ্ঞান দেখতে পাও, সে কীরকম?’
‘আরে না। সেরকম কিছু নয়। পুবের দেওয়ালে সব বই রাখা। কিছু খোলা, কিছু বন্ধ। সব পৃষ্ঠা আমার পড়া। ওকেই বলি জ্ঞান।’
‘কোনও কথা শুনতে পাও? কেউ কথা বলে ওঠে?’
‘আমার কান একেবারে ঠিক আছে ডাক্তারবাবু।’
‘হঠাৎ কোনও লোক দেখতে পাও? মনে হল, পাশে বসে আছে, কী কিছু বলে সরে গেল?’
‘আমার চোখও মোটের ওপর ঠিক আছে। তবে আমি বুঝতে পারছি আপনি জানতে চাইছেন আমি হ্যালুসিনেশন দেখি কি না। দেখি না। আপনি নিশ্চয় বলবেন না, ওই কুঠুরিতে আমার স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য রোজ সর্বাঙ্গাসন ও প্রাণায়াম করা উচিত?’
‘হ্যালুসিনেশন না দেখলেও তুমি অ্যাপোফেনিয়ায় ভুগছ। আমি তোমাকে আসনের পরামর্শ দিতে চাই না, তবে তোমাকে দিনে আধা ঘণ্টা মাঠে হাঁটার অনুমতি যাতে দেওয়া হয়, আমি দেখব।’
‘শেকল-বাঁধা অবস্থায়?’
‘সে তো থাকতেই হবে।’
‘আপনি আমার ঊরু সারিয়ে দিন। আমারই মাংসভুক কীট আমাকেই ছেয়ে ফেলছে, এটা হতে দেওয়া যায় না। এই দুর্নীতির বিরুদ্ধেই আমরা সক্রিয় ছিলাম। এখন আর সেসব প্রসঙ্গ তুলে লাভ নেই। শুনে রাখুন, আমি অ্যাপোফেনিয়ায় ভুগছি না, কারণ ওটা কোনও রোগ নয়। বিশেষ শৈল্পিক ক্ষমতা বলা যায়। যাদের অনুভব করার ক্ষমতা নেই তারা ভাবে পাগলামো।’
‘অ্যাপোফেনিয়া কাকে বলে জানো তুমি?’
‘আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে আমার মধ্যে যা সক্রিয় তার নাম প্যারিডোলিয়া। স্যাঁতা-পড়া দেওয়ালে আমি যদি রূপমঞ্জরীদের দেখতে পাই তার জন্য আপনি আমাকে ওষুধ দেবেন, আর ওই অসভ্য ম্যাগট, যারা আমারই খাচ্ছে আর আমাকেই চোখ রাঙাচ্ছে তাদের হত্যা করবার কোনও তাগিদ নেই?’
অবশেষে সে হাসপাতাল থেকে স্বক্ষেত্রে ফিরে এক সযত্ন কুটির পেয়েছিল যার আঙিনা পরিচ্ছন্ন, গোবরমাটি লেপন-করা দেওয়ালে গেরিমাটির সুন্দর আলপনা। উত্তরের দেওয়াল উত্তরার ভিজে ভিজে শরীরে নতুন নতুন বিভঙ্গে নতুনতর ছবি। পুবের দেওয়ালে এক পোঁচ কলিচুনের আস্তর। জ্ঞান মুছে দেওয়া উদ্দেশ্য নিশ্চয়। দক্ষিণের দেওয়াল বন্ধুর কোনও পরিবর্তন নেই। পশ্চিমে চে-লেখা মুক্তির দেওয়ালে আলকাতরা দিয়ে চে -কে গোল করে দেওয়া। বিছানা বালিশ কম্বল নতুনের মতো, যেমন নতুনের মতো তার দেহ ও পোশাক।
চে-কে কালো গোল্লা দেওয়ার উদ্দেশ্য সে বোঝার চেষ্টা করেনি। দাগা বুলোনো গভীর চে আলকাতরায় মোছা যায় না। আগুনে পোড়ানো যায় না। জলে ভাসানো যায় না। তবে হ্যাঁ, কালো দিয়ে তাকে দাগিয়ে দেওয়া যায়।
যে মানুষের মুক্তিদাতা, স্বয়ং মুক্তি, তার কালোই কী আর সাদা কী।
সেই সময় চিকিৎসক তাকে পাগল প্রতিপন্ন করতে ব্যর্থ হলে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেন, ওই দীনের কুটিরে সে যেন প্রত্যহ কিছুক্ষণের জন্য হলেও চলাফেরা করে। সে বলে, ‘শেকল খুলে দিন। চলব। ফিরব। ওই কুঠুরি থেকে কোথাও পালাব না। আমি পালাতে শিখিনি। পলায়ন ঘেন্না করি। যেদিন চে খুলে দেবে মুক্তির দুয়ার, সেদিন যদি কেউ বাধা দিতে আসে, আমি তাকে হত্যা করে মুক্তির ধ্বজা উড়িয়ে চলে যাব।’
‘শেকল খোলার আমি কেউ নই। আমার কাজ চিকিৎসা করা।’
‘সবাই তা-ই বলে। আমিও বলতাম। সিদ্ধান্ত নেবার আমি কেউ নই। আমি নির্দেশ পালন করি মাত্র। ঠিক আছে। আমি শেকল নিয়েই চলব, ফিরব, কুঠুরির এ মাথা থেকে ও মাথা। মাংসকীটের বসতি হতে দেব না নিজেকে।’