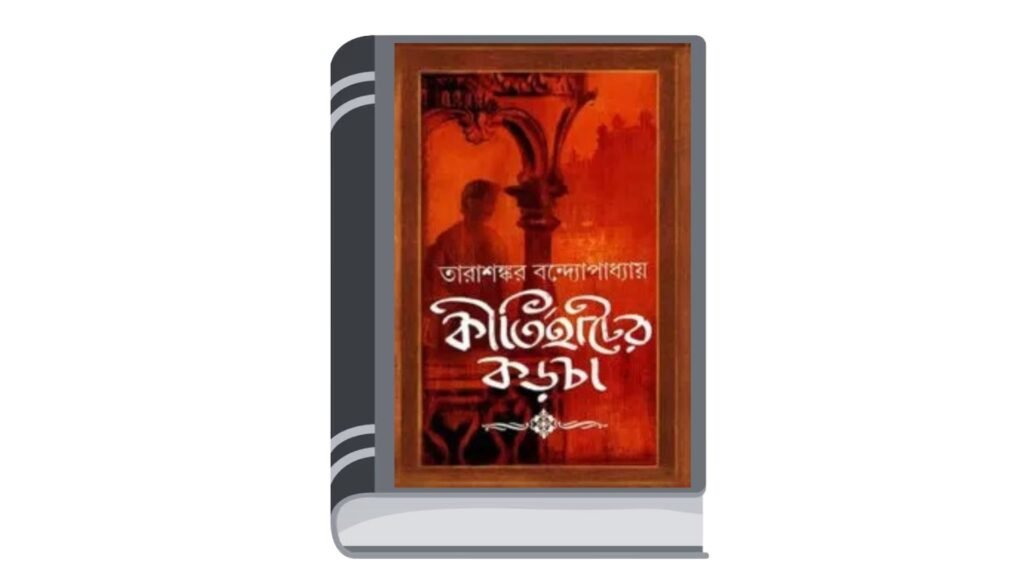কীর্তিহাটের কড়চা – ৩.২
২
কিছুই পেলাম না। দেবোত্তরের খাতার মধ্যে কোথাও পেলাম না ইমারৎ খরচ। আবার ওল্টাতে লাগলাম। এবার হঠাৎ চোখে পড়ল, একটা টাকা জমা হয়েছে সেইদিকে। সামান্য টাকা, দেড়শো টাকা জমা! মাঃ সোমেশ্বর রায়। দেবোত্তরের ইটের পাঁজা বিক্রয় হয়, সোমেশ্বর রায় অন্দরমহল তৈরীর জন্য খরিদ করেন—তস্য মূল্য বাবদ দেড়শত টাকা। চমকে উঠলাম। এই তো পেয়েছি! অর্থাৎ দেবোত্তর থেকে ইট নিয়েও তার দাম পর্যন্ত সোমেশ্বর রায় দিয়েছেন নিজের তহবিল থেকে। পুরো একগ্লাস হুইস্কি খেয়ে বেহালাখানা তুলে নিয়ে ভাবলাম বেহালা বাজাব। গভীর রাত্রি। আকাশে পশ্চিম দিকে চাঁদ পাণ্ডুর হতে সবে আরম্ভ করেছে। ছোটজাতের এক রকম পাখী আকাশে ক্রমাগত উড়েই বেড়াচ্ছে। সে পাখী তুমি বোধহয় দেখোনি সুলতা, কলকাতায় কাটিয়েছ তো সারা জীবন! ওরা চকোর। কাঁসাইয়ের ওপারের জঙ্গল থেকে কোন ফুলের গন্ধ আসছে। বউ-কথা-কও পাখীটাও ডাকছিল। গ্রাম নিস্তব্ধ। শুধু মধ্যে-মাঝে গ্রামের কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে চীৎকার করছিল। ছড়িটা তুলে নিয়ে টান দিয়েছি; বাজাব—’শুন যা শুন যা পিয়া’। তোমাকেই ভেবেছিলাম মনে মনে। হঠাৎ একটা দমকা বাতাস এল। জমাখরচের খাতাখানা খোলাই ছিল, ফরফর ক’রে ওল্টাতে লাগল। পুরনো কাগজ ছিঁড়ে যাবে ভয়ে ছড়িটা দিয়েই চেপে ধরলাম এবং বেহালাটা রেখে বন্ধ করতে গেলাম।
হঠাৎ নজরে পড়ল পাতাটায় লেখা—সৎকার খরচ; ঠাকুরদাস পাল খুন হওয়ায় তাহার লাশ সদরে যায়; সদরে লোক পাঠাইয়া তাহার শবদেহ সৎকারের খরচ, পঁচাত্তর টাকা। তার জায় রয়েছে—বারবরদারি যাতায়াত খরচ, তাহাদের খাদ্য খরচ, চন্দন কাষ্ঠ, ঘৃত, নূতন বস্ত্ৰ ইত্যাদি খরচ। ঠাকুরদাস পাল! সেই ঠাকুরদাস! সে খুন হয়েছে। তার সৎকারে চন্দন কাষ্ঠ ঘৃত খরচ করেছেন রত্নেশ্বর রায়।
আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম। ওল্টাতে লাগলাম। ঠাকুরদাসের শ্রাদ্ধের খরচ পেলাম। সেই পৃষ্ঠাতেই পেলাম পিদ্রু গোয়ানের পরিবারকে সাহায্য।
একটা আশ্চর্য চেহারা ফুটেছিল রত্নেশ্বর রায়ের। মাথাটা নত হয়ে এল। আক্রোশ ক্ৰোধ তাঁর চিত্তকে দৃষ্টিকে অভিভূত করতে পারেনি। ঠাকুরদাসকে যে খুন করেছে তার অপরাধে তুমি তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে অপরাধী করোনি।
উলটেই গেলাম খাতা। হঠাৎ একটা চার অঙ্কের খরচ চোখে পড়ল। পনেরশো টাকা। খরচের বিবরণ পড়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। হুজুর বাহাদুরের পত্রের আদেশ অনুযায়ী পিছু গোয়ানের দায়রা মামলায় তাহার পক্ষ সমর্থনের জন্য এক জায়গায় খরচ—পনেরশো টাকা!
চমকে গেলাম।
প্রতিটি পাতায় রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের সই রয়েছে। বিশ্বাস করতে পারলাম না। পিদ্ধ গোয়ানের দায়রা মামলায় পনেরশো টাকা সাহায্য? তার পরিবার সন্তান-সন্ততিদের সাহায্য করেছেন বুঝতে পারলাম। দয়া করুণা! এও কি দয়া? করুণা? গোয়ান মেয়েটি কি এসে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়েছিল—বাঁচাও হুজুর! বাঁচাও আমার স্বামীকে! না—? সন্দেহ হচ্ছিল রত্নেশ্বর রায়ের মত ব্যক্তিকেও।
সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল শ্যামনগরে চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারি আছে—ঠাকুরদাস দাতব্য চিকিৎসালয়। মনে মনে প্রণাম করলাম রত্নেশ্বর রায়কে, বললাম—ক্ষমা কর আমাকে।
সারাটা রাত মদের নেশাতেও ঘুম আসেনি।
.
সকালবেলা স্নান ক’রে নেশাটা কেটেছিল, কিন্তু রত্নেশ্বর রায়ের চরিত্র নিয়ে যে ঘোরটা লেগেছিল সেটা কাটেনি। মনের মধ্যে একটি কথাই ধ্বনিত হচ্ছিল—অদ্ভুত! অদ্ভুত!
চা খাচ্ছিলাম এমন সময় আমার কর্মচারী এসে ডাকলে —বাবু, বুঝারত আরম্ভ হয়েছে। গ্রামের নৈঋত কোণ থেকে। এসে পড়ল বাড়ীর সীমানায়। ওরা বাড়ী দেবোত্তর বলে আপত্তি দেবে।
—ঠিক আছে চলুন। ডিকুকে বা রোজারিওকে ডাকুন। খানকয়েক খাতা নিয়ে যেতে হবে। বাড়ীতে আসতে দেরী ছিল। নায়েব শঙ্কিত হয়ে ছুটে এসেছিল। নৈঋত কোণ থেকে উত্তর দিকে সেটেলমেন্ট চলছিল। সাহেব টেবিলের উপর ম্যাপ গেঁথে তা থেকে প্লট বাই প্লট বুঝারত করে চলেছিলেন। লোক অনেক জমেছে। গ্রামের বর্ধিষ্ণু ব্যবসাদার সুরেন দে, রাধাগোবিন্দ ভট্টচার্জ, শিবনাথ ওঝা, নটবর সিং, নন্দ ঘোষ, নটু বাউড়ী, মোটা কালো ইব্রাহিম শেখ, তা ছাড়া ধনেশ্বর, প্রণবেশ্বর এঁরা তো আছেনই।
সাহেব গম্ভীরকণ্ঠে বললেন—এতক্ষণে সময় হল আপনার?
—তাতে আপনার কাজে ব্যাঘাত হয়েছে?
—নিশ্চয় হয়েছে। আপনারা জমিদার। প্রজা যে স্বত্ব বলছে সে সম্বন্ধে আপনাদের সম্মতি কিংবা আপত্তি দুটোর একটা চাই। না হলে আমার কাজ শেষ হয় না। ওগুলোতে আপনার মতামত কিছু নাই তাই আমি লিখেছি। মানে প্রজার পক্ষেই গেছে। এঁরা আপত্তি দিয়েছেন। লিখেছি। এটাতে কি বলুন?
তবুও বুঝতে পারলাম না। সবে তো পনের বিশ দিন গেছে। প্রজাইস্বত্বের ব্যাপার ঠিক রপ্ত হয় নি।
হঠাৎ পিছনে একটা দুর্বোধ্য হাউহাউ শব্দ শুনলাম। সকলেই ফিরে তাকালে। দেখলাম, একজন বৃদ্ধ, লোলমাংস থলথল করছে, তার মধ্যে হাড়গুলো প্রকট হয়েছে, মাথায় চুল উঠে গিয়ে যে ক’গাছা আছে তা সাদা ধপধপে এবং ব্যোমকেশের মত ঊর্ধ্বমুখী, একমুখ খোঁচাখোঁচা দাড়িগোঁফ, ভুরু দুটোও পাকা এবং ঘন মোটা। পরনে হাঁটু পর্যন্ত ধুতি, একজন তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী ফিটফাট পোশাকপরা ভদ্রলোকের হাত ধরে আসছে। চোখে দৃষ্টি নেই, ঘোলাটে চোখের তারা দুটো শূন্য-লোকের দিকে স্থির নিবদ্ধ, পা দুটো ঠিক পড়ছে না। লোকটা হাউহাউ করে কি বলছে তা বোঝা যাচ্ছে না।
অফিসার বিরক্তিভরে তাকালেন। বললেন—চীৎকার করো না এমন কর!
বৃদ্ধের সঙ্গের ভদ্রলোকটি খাসা ইংরিজীতে বললেন—তার নিজের কথা বলবার অবশ্যই স্বাধীনতা আছে।
হাকিম চটে উঠে বললেন—কে তুমি? ওই ই বা কে?
ভদ্রলোক বললেন—ওঁর নাম বহুবল্লভ পাল। উনি এইখানকার বিশ দাগ প্লটের মালিক। আমি ওঁর ছেলে, উনি চোখে দেখতে পান না, সঙ্গে নিয়ে এসেছি। ইংরিজীতেই বললেন। উরু ভটচাজ, সে প্রৌঢ় লোক, বিচিত্র-চরিত্র মানুষ বলে পরিচয়টা শুনেছিলাম সুলতা, কিন্তু প্রত্যক্ষ পরিচয় বিশেষ ছিল না। শুনেছিলাম প্রথম যৌবন থেকে মেজঠাকুরদার থিয়েটারে পাঠ করতেন, তারপর প্রেম করে একটি শুদ্রকন্যাকে নিয়ে কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন। বাড়ীর জমি বিক্রী করে কিসের দোকান করেছিলেন, তারপর ফেল পড়ে গ্রামে ফিরে বিয়ে করে রায়বাড়ীতে চাকরীও করেছিলেন। এখন গ্রামে মাতব্বরী করেন। ক্রিয়াবাড়ীর যজ্ঞে উরু ভটচাজ অপরিহার্য। তিনি রান্নাশালে মোড়া নিয়ে বসেন। বাঁ হাতে সিগারেট পোড়ে ডান হাতে হুঁকো থাকে। কোন নেশা নেই এ ছাড়া। ওই খেয়েই ক্রিয়া শেষ করে উঠে যান। তবে এখনও নাকি ব্রাত্যপাড়া থেকে গোয়ানপাড়া পর্যন্ত মেয়েদের কাছে প্রিয়জন। তার জন্য কিন্তু তিনি লজ্জিত নন। কথাবার্তা খুব ভাল বলেন, অবশ্য তার একটা বিশেষ ধরন আছে। উরুবাবু বলে উঠলেন—ব্রিলিয়ান্ট স্টার অব আওয়ার ভিলেজ স্যার। উজ্জ্বল নক্ষত্র। এম.এ.-তে ভাল রেজাল্ট করেছে। আমাদের বহুবল্লভ পালের ছেলে। শ্রীরাধাবল্লভ পাল। উকীল হয়েছেন।
হাকিম বললেন—নরম সুরে বললেন—বেশ তো, কি বলতে চান সেইটে তো পরিষ্কার ক’রে বলতে হবে।
রাধাবল্লভ বললেন—উনি বলছেন এসব হল লাখরাজ।
এবার ধনেশ্বর এগিয়ে এসে বললেন—না। ওগুলি জোতের সামিল।
—এ্যাঁ? জিজ্ঞাসা করলে বহুবল্লভ।
কানের কাছে মুখ এনে ছেলে বললে—ধনেশ্বরবাবু বলছেন—না। এ সব জোতের সামিল। রায়তি স্থিতিবান!
—না। চীৎকার করে উঠল বহুবল্লভ।
হাকিম বললেন—বেশ তো, কাগজ দেখান। লাখরাজ তার প্রমাণ তো দিতে হবে! -án?
কানের কাছে মুখে রেখে ছেলে বুঝিয়ে দিলে। তাতে পাল বললে—কখুনও খাজনা আমি দিই নাই! কখনও না! আমার বাবার আমল থেকে। হ্যাঁ!
উকীল বললেন-ভোগদখলসূত্রে নিষ্কর।
হেসে হাকিম বললেন—নিশ্চয় লিখব। তার সঙ্গে ধনেশ্বরবাবুদের আপত্তিও রেকর্ড করতে হবে আমাকে।
—ধনেশ্বরবাবু! আহা-হা! চিৎকার করে উঠল বহুবল্লভরায়বংশের মুখ উজ্জ্বল করছে। বাহবা বাহবা।
ধনেশ্বর বললেন—বহুবল্লভ, তোমার ধন হয়েছে, ছেলে এম.এ. পাস করেছে, না? তবুও কথাটা হিসেব করে বলো। বুড়ো হাতী করতে মরতেও সে হাতী। সেকাল হলে—।
বহুবল্লভের উকীল ছেলে বললে-ড্রোনস অব দি সোসাইটি! লজ্জাও নেই এদের! প্রণবেশ্বরের মুখ লাল হয়ে উঠেছিল, সে বললে—এর মধ্যে ঝগড়ার তো কোন কারণ নেই। বহুভ যা বলেছে—
—প্লীজ, সে বহুবল্লভবাবু! উকীল বললে।
—বহুবল্লভবাবু?
—হ্যাঁ, না বললে উনিও নাম ধরে বলবেন!
—বেশ। যে যা বলছে তাই রেকর্ড করুন আপনি স্যার।
বহুবল্লভ তবু থামল না। সে হাউহাউ করে বললে—কীর্তিহাটে বসতবাড়ী আর গোচরের খাজনা মাফ ছিল। কখনও জমিদার লেয় নাই, পেজাতে দেয় নাই। মাফ করেছিলেন সোমেশ্বর হুজুরের পিতা কুড়ারাম হুজুর। আজ পাঁচপুরুষ আমাকে নিয়ে ভোগ করে আসছি। ই আমাদের
স্বত্ব হয়েছে। আজ লোব বললেই দোব আর জমিদার পাবে? এইটো হাকিমের বিচার?
হাকিম এবার নিজেই চীৎকার করে বললেন –বিচার আমি করব না। সে পরে হবে। আমি রেকর্ড করে যাব, যা প্রমাণ পাব সব!
হঠাৎ মনে পড়ে গেল আমার সুলতা, রায়বংশের পাঁচালী।
কীর্তিহাটে বাস্তু জমি গোধন চারণ ভূমি
মা কালী চরণে নমি দিলাম নিষ্কর
মাঠেতে পুকুর খুঁড়ি সিচ নিম্ন তিন গাড়ি
মৎস্য খাবে লোকে ধরি রুই কাৎলা পর।
আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম- আমার কথাটা লিখে নিন।
—আপনার আবার ভিন্ন কথা আছে নাকি?
—আছে। ধনেশ্বর-কাকা বোধহয় জানেন না। না-হলে আপত্তি দিতেন না। বহুবল্লভ পাল যা বলেছেন তা সত্য। কীর্তিহাটে বাস্তুজমি গোচর নিষ্করই বটে। কুড়ারাম রায়-ভটচাজমশাই দিয়ে গেছেন। তার সঙ্গে মাঠের পুকুরের সিচ এবং রুই কাৎলা ছাড়া মাছও সাধারণ লোককে ধরে খেতে দিয়ে গেছেন।
—তার নজীর চাই হে। তার নজীর চাই।—গম্ভীর ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন ধনেশ্বরকাকা।
আমি বললাম-আছে নজীর। দেখাব। কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিজের জীবনের পাঁচালী আমি পেয়েছি, আমি পড়েছি, আমি দেখাব।
সকলে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বৃদ্ধ বহুবল্লভ বার্ধক্যজড়িত কণ্ঠে প্রায় চীৎকার ক’রে বললে—পেনাম! পেনাম। তোমাকে পেনাম বাবু! কই তুমি কই! রাধা! বাবু কই? নিয়ে চল কাছে
ছেলে হাত ধরে বৃদ্ধকে কাছে নিয়ে এল। সে আমার হাত ধরলে প্রথম। তারপর হেঁট হতে গেল, আমি বাধা দিলাম।
—না। বয়সে আপনি অনেক বড়।
—বয়সে বড়? তুলসীপাতা তুমি বাবু। নিখুঁত বেলপাতা। পোকালাগা চক্রলাগা পাতা ফেলে দিতে হয়। ওই ধনেশ্বরবাবুদের মত। তুমি নিখুঁত। মাথায় করতেই হবে গো। পেনাম না লাও, নমস্কার লাও! কই, মুখে একবার হাত বুলিয়ে দেখি!—হ্যাঁ, বটে। বেশ লম্বা গো। লাগাল পেতে বেঁকা কোমর সোজা করতে হয়। নাক টিকলো। চামড়া মাখনের মত! বা বা বা! গোটা গাঁয়ের লোক আশীর্বাদ করবে তোমাকে। তোমার ঠাকুরদাদার বাবা রায়বাহাদুরকে দেখেছি আমি। ছেলে-মানুষে। ঠাকুরদাস পালের পেথম পক্ষ মারা গেলে আমার পিসীর সঙ্গে রায়বাহাদুর তার পেয়ারের ঠাকুরদাস পিসের বিয়ে দিয়েছিল গো। তিনি ছিলেন এক জবর লোক! তুমি তার বংশের ছেলে বটে।
হয়তো কিছুটা নাটুকেপনা আমার মধ্যে আছে সুলতা। আমি ভেবে দেখেছি। নইলে ওইভাবে রাত্রে চীৎপুরে দেহ-ব্যবসায়িনীদের দান করে রূপকথার রাজপুত্র সাজতে চাইব কেন? নাটুকেপনা বলতে পার আবার অভিজাতপনা বলতে পার। আবার রায়বংশের ধারাও বলতে পার। আমাকে সেদিন সেটেলমেন্টের সাহেব ঠাট্টা করেছিল। আমি যে মাত্র ওই পাঁচালীর কথা বললাম এবং বললাম—ভোগদখলকারীদের লাখরাজ দাবীতে আমার আপত্তি নেই, অমনি তার ক্রিয়া একটা হয়েছিল। যেটার জন্যে বহুবল্লভ পাল প্রবল উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলে! যে কথার পিঠে বা জবাবে ধনেশ্বর-কাকার দল একেবারে চুপ ক’রে গেল—কোন কথা বলতে পারলে না। কিন্তু সায়েব কথা বললেন—বেশ অ্যাক্টিং করার মত ভঙ্গি, প্রচ্ছন্ন শ্লেষ মিশিয়ে বলে উঠল—দেখুন—দেখুন- আপনাদের জমিদার সাড়ে আট আনার মালিক—কি মহান সত্যবাদী দেখুন!
বাড়ি এসে একটা আশ্চর্য তৃপ্তির মধ্যে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। কলকাতার মাথায় আকাশ অবশ্যই আছে—কিন্তু সে আকাশ মানুষের চোখে বড় পড়ে না। আমি ঝড়ের আকাশ দেখতে ছাদে উঠতাম। রাত্রে নক্ষত্র দেখতে উঠতাম কিন্তু কখনও সাধারণ সময়ে খোলা আকাশের দিকে ভরপুর মন নিয়ে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে থাকি নি। সেটা এখানে এসে আমাকে পেয়ে বসেছিল। এখানে আকাশের একটা রঙ আছে। ঋতুতে ঋতুতে পাল্টায়। সেদিন আকাশটা ছিল ঘষা কাঁচের মত। মানে ধুলো উঠেছিল বাতাসের স্তরে। তারই উপরে খাঁ-খাঁ করা আকাশে একজোড়া বড় আকারের কালচে রঙের পাখী–দুটি ডানা স্থিরভাবে মেলে দিয়ে পাশাপাশি উড়ে আসছিল। পক্ষীমিথুন তাতে সন্দেহ নেই। কল্পনা করছিলাম—তোমাকে নিয়ে এই বিবিমহলে জীবনটা এইভাবে স্থির পাখা বিস্তার করে ভেসে থাকার মত কাটিয়ে দেব। জমিদারী, বিবিমহল, রায়বাড়ি এ-সবের উপর আমার আকর্ষণ তো ছিল না, সে তুমিই সাক্ষী দেবে, কিন্তু সেদিন ঘোর লেগেছিল। বহুবল্লভের প্রণামের অনেক দাম। ওর উকীল ছেলে আজ মুখ টিপে হাসলেও কাল আমার কাছে নত হবে। ওকেই না হয় এখানে ম্যানেজার রাখব। নতুন উকীলের আর কত উপার্জন, উকীল ম্যানেজারের একজন দরকার হবে।
পারমানেন্ট সেটেলমেন্টের আগে থেকে জমি নিয়ে আইন বদলাতে বদলাতে উনিশশো পঁয়ত্রিশ মহাভারত হয়ে উঠেছে। বেঙ্গল টেনেন্সী এ্যাক্টের আয়তন দেখলে চমকে উঠতে হয়। পঞ্চম আইন, ষষ্ঠ আইন, সপ্তম আইন, অষ্টম আইন এসব সেকালের। তখন প্রজাকে এনে আটক কয়েদ ক’রে খাজনা আদায় করতে পারত জমিদারেরা। তারপর মাঠে ধান ক্রোক করে আদায় করতে পারত খাজনা। সেই আমলে সোমেশ্বর রায় বীরেশ্বর রায় জমিদারী করে গেছেন। তারপর ওসব আইনের অষ্টম আইন বাদে সব উঠে গেছে। জমিদারপ্রজার মধ্যে সরকারের চোখে ভেদ নেই। এখন সব মুনসেফী সাবজজ কোর্টের এলাকার বিচারের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। আদায়-তহশীল সেরেস্তা থেকে মামলা সেরেস্তা বড় হয়ে উঠেছে। এখন একজন উকীল রাখলে মন্দ হয় না। ভেবেছিলাম বিকেলে লোক পাঠাব।
হঠাৎ এরই মধ্যে কি করে ঠাকুরদাস পাল উঁকি মেরে মুখ বাড়ালে বলতে পারব না। ঠাকুরদাস পাল —বহুবল্লভের পিসেমশাই হত।
বহুবল্লভ তো বলতে পারবে ওই কথাটা! ঠিক করলাম নিজেই যাব বিকেলে বহুবল্লভ পালের কাছে।
দুপুরে মেজঠাকুমা এসেছিলেন—তাঁকে বললাম কথাটা। মেজঠাকুমা আশীর্বাদের ছলে অনেক গুণগানই বল আর বাস্তব গানই বল করতে করতে ঘরে ঢুকেছিলেন। তিনি বললেন—সারা গ্রামে ধন্যি ধন্যি উঠেছে।
কথাটা চাপা দিয়ে আমি বহুবল্লভের ওখানে যাবার কথা বললাম। তিনি খুঁতখুঁত করলেন প্রথমটা। তারপর বললেন—তা যাস্। শুনেছি আমার শ্বশুরের হুকুম ছিল আমার শাশুড়ীর উপর। বিকেলে তিনি বের হতেন ঝি আর চাকর নিয়ে। বিশেষ করে বাউড়ী বাগদী চুয়াড় পাড়ায় তিনি গিয়ে দেখতেন কার বাড়ীর চাল থেকে ধোঁয়া উঠছে কার উঠছে না। মানে কার রান্না চেপেছে কার চাপেনি। বাড়ী থেকে চাল যেত তাদের বাড়ী। ভদ্র শূদ্র গরীব কারুর অসুখ বেশী শুনলে খোদ কর্তা যেতেন দেখতে-চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে। তা যেতে পারিস। সঙ্গে লোক নিয়ে যাস।
মেজাজটা যাকে জমিদারী ভাষায় ‘সরি’ বলে তাই হয়ে গেল। বিকেলে গেলাম বহুবল্লভের বাড়ী। সদগোপ পাড়া মাটির দেওয়াল-কোঠাবাড়ী খড়ের চাল ঘর। রাস্তা সঙ্কীর্ণ, একখানা গরুর গাড়ী যায়। বহুবল্লভের ঘরের চালে টিন। পোঁতা বা ভিত বাঁধানো। বাড়ীর সামনেটার পাকা থাম দেওয়া পাকা মেঝে। পাল চোখে অন্ধ হলেও শনের গোছা টাঙিয়ে ঢেঁড়ার পাক দিয়ে দড়ি কাটছিল। তকলীতে সূতা কাটার মত! বসেছিল একখানা তক্তাপোশের উপর উপু হয়ে।
আমার সঙ্গে মানে পিছনে লোকও জুটেছিল—দুটো কুকুরও চেঁচাচ্ছিল। আমি সামনে দাঁড়িয়ে বললাম-পালমশাই, আমি আপনার কাছে একবার এলাম!
দৃষ্টিহীন চোখ সামনে তুলে পাল বললে-কে? তারপর আমার কাপড়জামা এবং ল্যাভেন্ডার সাবানের গন্ধ শুঁকে বললে—হাকিম মশায়—
—না। আমি সুরেশ্বর রায়।
—আঁ! চমকে উঠল পাল। তারপর চীৎকার করে বললে—ওরে রাধা। ওরে অ রাধা! গেলি কোথা রে বাপু?
আর একজন প্রবীণ এসে দাঁড়াল এবং নমস্কার করে আমাকে আহ্বান করে বললে—আসুন আসুন। বলে ঘর থেকে দেশী ছুতোরের হাতে শালকাঠের তৈরী ভারী চেয়ার এনে পেতে দিয়ে বললে-বসুন।
পাল বললে—কে? বেজো না কে?
—হ্যাঁ।
—রাধা কোথা? রাধা!
—সে হাকিমের কাছে গিয়েছে।
—হাকিমের কাছে? কচু-পোড়া খেয়েছে—নিকাপড়া শিখে উকীল হবে! হাকিম ছাড়া আর চিনলে না কিছু! রসুন বসুন বাবা, বসুন। আজ সমস্তদিন তোমার নাম করেছি গো!
—আমি একটা কথা জানতে এসেছি আপনার কাছে।
—ওই আমবাগানটার আর পুকুরটার কথা! ওটোতে বাবা কিছু গোল আমাদের আছে। ওটো রায়বাহাদুর আমাদিগে দানটান করেন নাই। যখন আমার পিসীর বিয়ে হয় উনিই খুব ধরে পড়ে বিয়ে দেয়ায়েছিলেন। পিসী আমার ডাগর হয়েছিল। বারো বছর বয়স্কম হয়েছিল। তা তখন পিসের বয়স আমার, তা পঁয়তিরিশ হবে বইকি! একটুকুন বেমানান হয়েছিল তো!—তা আমার ঠাকুরবাবা—রায়বাহাদুরদের কথা মেনে বিয়ে দিয়েছিল। ত্যাখন ওই বাগান আর মওল পুকুর ঠাকুরবাবাকে ভোগ করতে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—ভোগ কর তু। কিন্তু গাছ কাটতে পাবি না—, পুকুরের মাছ খাবি—কিন্তুক পুকুর বাগান বেচতে পাবি না। এই বিত্তান্ত বটে মশায়। দেখ বাবু, তুমি আজ এমুনি করে সত্যি কথা বললে—আমি মিছে কি ক’রে বলি?—
আমি বললাম- না, ওর জন্যে আমি আসিনি।
চোখ স্থির ক’রে পাল বললে—তবে?
—আমি কয়েকটা কথা জানতে এসেছি ঠাকুরদাস পাল সম্পর্কে।
—অঃ। তিনি মহাশয় লোক ছিলেন গো। যেমন দ্যাহ তেমনি ক্ষ্যামতা আর তেমুনি সাহস। দুদ্দান্ত সাহস—দুদ্দান্ত লোক। আপনকার ঠাকুরবাবার বাবা রায়বাহাদুরের চেলা গো! আর আরও ছিল-কমলদাদা অন্তপান। তোমার ঠাকুরবাবার বাবার পেথম নাম তো কমলাকান্ত। মামা পুষি নিয়ে নাম দিলে রত্নেশ্বর। অঃ শুনেছি, আমরা তো তখন জন্মাই নাই। মামা ভাগ্নেতে সে ভয়ানক ঝগড়া। বলে—মামা গুলী করতে গিয়েছিল ভাগ্নেকে। সেই তো ঘরে আগুন লাগল পিসেদের গাঁয়ে। তাতে তোমার ঠাকুরবাবার বাবাকে বাঁচাতে ছুটল পিসে, বাঁচালে, ইদিকে পিসের প্রথম সংসার জ্বলন্ত চালচাপা পড়ল। আবার শেষটায় যে কি হল—
—কি হল—তাই জিজ্ঞাসা করতে এসেছি আপনাকে।
—সেটাতে পিসের দোষই বটে। বুয়েছেন—ঠিক কথাটি কেউ জানে না। সি কাক পক্ষীতেও না! তবে—দোষ পিসের বটে। ক্যানে বলছি—শোনেন। পিসের ছেলে আমাদেরই হামজুটি—এই বছর তিন চারের বড় হবে। সি থাকত কীর্তিহাটে। থাকত আপনকার ঠাকুরবাবা —দেবেশ্বর বাবুমহাশয়ের কাছে। হ্যাঁ, তিনি একটা বাবুমহাশয় বটে। চেহারায় যেমন কার্তিক, তেমনি মেজাজ। ইংরিজী নেকাপড়াতে পণ্ডিত। বাঘ মারতে যেতেন। ঠোঁট বেঁকিয়ে একটা হাসি ছিল তাঁর। সি মশায় ছুরির মতন। বুয়েছেন। আমার দাদা ঠাকুরদাস পিসের বড় বেটা তাঁর কাছেই থাকত। কলকাতা গেলেন বড়বাবু, সেও কলকাতা গেল। তাকেও পড়াতে চেয়েছিলেন রায়বাহাদুর। তা তার হল না। লেখাপড়া ছেড়ে ওই বড়বাবুর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করত। শিকারে যেত। তা পরেতে দুম্মতি—গোয়ানপাড়ার পিজ গোয়ানের বুন ছিল—তার নাম ছিল ভায়লা। মশায় সে এক মেয়ে বটে। যেমন রঙ তেমনি চেহারা। সি দেখেছি আমরা। তাকেই সে বার করে নিয়ে ভাগলো। এইতে পিজ খুব থাপ্পা। একে গোয়ান তার উপর ছিল মারহাট্টা গুন্ডা ডাকাত। সে রায়বাহাদুরের কাছে নালিশ করলে। রায়বাহাদুর ঠাকুরদাস পিসেকে বললে—তোর ছেলেকে সাজা নিতে হবে। কি হল ঠাকুরদাস পিসের—সে বললে—সাজা কিসের? সে বেটাছেলে। মেয়েটার বিচার কর। দেখ সেই হারামজাদী আসলে দোষী। রায়বাহাদুর খুব ধমকালে। মশায় –সেদিন সেখানে সে ঘরে মাছি ঢুকবার হুকুম ছিল না। ছিল পিসে, পিভ্রূ আর খোদ রায়বাহাদুর নিজে। পিসের দুম্মতি—সে বললে—তা হলে আমিও সব ফাঁস করে দোব হ্যাঁ। কি ফাঁস করে দেবে, কি বিত্তান্ত তা কেউ জানে না মশায়, জানত পিসে, জানতেন রায়বাহাদুর। তা লোকে অনুমান করে মশায় যে রায়বাহাদুরের সঙ্গে তার বুন মামলা করেছিলেন, জানেন তো। মানে রায়বাহাদুর পুষ্যবেটা আর মেয়ে হল আসল। রায়বাহাদুর মামলা করেন নাই, টাকা দিয়ে মিটিয়েছিলেন। সেই তারই কোন গুহ্য কথা বোধ হয় হবে। তাই ফাঁস করে দোব বলে পিসে বেরিয়ে এসে পিভ্রূকে বললে—আয় শালা গোয়ান ওর বিচার রায়বাহাদুর করবে কিরে, তোতে আমাতে হোক। আয়। এই তখুনি রায়বাহাদুর ইশারা দিয়ে থাকবেন। তাই পিদ্রু বেরিয়ে এল, দুজনে হাতাহাতি করতে করতে নদীর ঘাট পর্যন্ত গেল। খাটটার নাম গোঘাটা। মানে ওই গোচরের পাশে তো। যেটা নাখরাজ ছিল আপুনি স্বীকার করলেন। ওই ঘাটে গরুতে জল খেতো। এখন লোকে বলে গোঘাটা মানে গোয়ানঘাটা! পিসে যেছিল ওই গোয়ানপাড়াতেই। মেয়েগুলোর সঙ্গে ভজিয়ে দেবে ভায়লার দোষ। বলছিল সে তাই—আয় তোদের বিটী গোলার কাছে শোন কার দোষ। কিন্তু ওই ঘাটে গিয়েই পিদ্রু একবারে এই এক হাত লম্বা ছোরা বার করে আচমকা দিলে বসিয়ে পিসের বুকে। অঃ, সে ঘড়া ঘড়া রক্ত পড়েছিল!
একটু চুপ করে থেকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—পিদ্রুর মামলায় অনেক টাকা খরচ হয়েছিল—
—হ্যাঁ। বড় উকীল দিয়েছিল। সে রায়বাহাদুর দিয়েছিলেন, তাই গুজব মাশায়।
—কেন?
—ক্যানে? একটু চুপ করে থেকে পাল বললে—সঠিক বলতে তো পারব না। এতবড় নোকটা-ধার্মিক নোক—কীর্তিমান নোক—সন্দেহ করলে পাপ হয়। নোকে বলে—দোষ তো পিসের বেটার। পিদ্রর অপমান তো পিসের বেটাই করেছে। ঝোঁকের মাথায় করেছে। এই বলে দয়া হয়েছিল তার। আবার দুচারজন বলে মাশায়, ওই যে পিসে বলেছিল, আমিও তাহ’লে ফাঁস করে দোব তাই জন্যে রায়বাহাদুর পিদ্রকে হুকুমই দিয়েছিলেন—দে সাফ করে!
কথাটা মনে লেগেছিল আমার সুলতা। এটাই সম্ভব। একটু চুপ করে থেকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম-ঠাকুরদাস পালের কে আছে বংশে?
পাল বলেছিল—পিসের ছেলের ছেলের ছেলে, মানে ছেলের নাতি আছে। সে এখন মস্ত লোক, ব্যারেস্টার সাহেব। সে জাতকুল এখানকার সব ঘুচিয়ে মুছিয়ে সাহেবী কাণ্ড। পিসের ছেলে ভায়লাকে নিয়ে কলকাতা পালিয়েছিল। বাবা খুন হল, রায়বাহাদুরের ভয়ে এল না। পিসী ছাদ্দ-টাদ্দ করলে। উদিকে তোমার ঠাকুরবাবার কাছে টাকা কিছু নিয়ে সে কলকাতায় ব্যবসা করলে। ভায়লাকেও ছেড়ে দিলে। এখানে বিয়ে ক’রে গিয়েছিল, সে বউ লিলে না। বউটার ভাগ্যি ভাল মরেও গেল। ত্যাখন সে করলে কি, বেক্ষ হয়ে গেল মাশায়। তখন বেক্ষ হওয়ার খুব ধুম হল। বিয়ে করলে বেক্ষবাড়ীতে। অবস্থা তখন ভাল করেছিল। তারপরেতে ভগবানের মার। ব্যবসা ফেল হ’ল। একবারে ফেল হল। ধাক্কাটা সইতে পারলে না। মরেও গেল। বউ ছেলে কোথায় যাবে, গেল বাপের বাড়ী। তারপরেতে ছেলে লেখাপড়া শিখে উকীল হল। লাতি বিলাত গেল। ব্যারেস্টার হয়ে এল। মস্ত লোক এখন। তবে শুনেছি নাকি গুজব বটে মাশায়—ওই ছেলের সব খরচ মায় লাতির বেলাত যাবার খরচ সে সব রায়বাহাদুর দিয়েছিলেন। না হয় তোমার ঠাকুরবাবা মানে বড়বাবু দিয়েছিলেন। দেবেশ্বরবাবু মহাশয়। তারা আর এখন পাল লয়। ঘোষ হয়েছে। মিস্টার রমেশচন্দ্র ঘোষ ব্যারেস্টার!
আমি চমকে উঠলাম। সুলতা, মনে হল কংসাবতীতে প্রলয় বন্যা এসেছে, সেই বন্যায় আমরা দুজনে দুদিকে ভেসে যাচ্ছি। তবুও মনে আশা করেছিলাম, ঐ রমেশ ঘোষ তোমার বাবা নন। কিন্তু সন্দেহ রইল না, পালের ছেলে উকীল ফিরে এসে যে ঠিকানাটা দিলে সেটা তোমাদেরই।
আবার আমি রায়বংশের অতীতের অন্ধকারের মধ্যে অন্ধের মত ছুটলাম, কোথায় আলো কোথায় আলো বলে। আলোর বদলে আগুনের কুণ্ডতে প’ড়ে যদি ছাই হয়ে যাই তাও এ থেকে ভালো।
.
হঠাৎ দিন চারেক পর কৃষ্ণযবনিকা যেন তুলে দিলেন ভাগ্যবিধাতা। হঠাৎ এল ব্রজেশ্বর। মনে আছে ব্রজেশ্বরকে, যে আমার নামে পরিচয় দিয়ে যেতো আসতো শেফালির বাড়িতে? যে আমাকে বলত রাজাভাই। সেই অতি মিষ্টমুখ, বাক্যবিদ সুন্দর চেহারা ব্রজেশ্বর। ধনেশ্বরকাল বড় ছেলে। যে অতি চতুর রায়বংশধরটি আমাকে মূর্খ প্রতিপন্ন করেছিল, সেই ব্রজেশ্বর? মনে আছে? হ্যাঁ, সেই হঠাৎ এল কীর্তিহাটে। তার আসার ভঙ্গিও বিচিত্র।
তখন আমি অন্ধকারে অন্ধের মত কাগজের স্তূপের মধ্যেই ডুবে আছি। কিন্তু সেটা বিষয় বা সম্পত্তির জন্য নয়। ওরা বাড়ির স্বত্বে আপত্তি দিয়েছিল। বলেছিল, এ কারুর ব্যক্তিগত নয়। এ দেবোত্তর। এজমালি অবিভাজ্য।
আমি সেই খাতাখানা দেখিয়েছিলাম। দেবোত্তরের খাতায় ইটের পাঁজা অর্থাৎ ভাটা বিক্রয় দরুণ জমা। শ্রীল শ্রীযুক্তবাবু সোমেশ্বর রায় মহাশয়ের অন্দরমহল তৈয়ারীর জন্য দেবোত্তরের যে ইটের ভাটা হইতে ইট লয়েন তাহার মূল্যবাবদ জমা মা: শ্রীল শ্রীযুক্ত সোমেশ্বর রায় মহাশয়। টাকাটা সামান্য, সাড়ে তিনশো টাকা।
ওরা চমকে গেল। দেখলে। তারপর আর কথা বললে না, আপত্তিটাও তুললে না। বুঝলাম ব্যক্তিগত জমাখরচের খাতাখানা ওদের হাতেই আছে। কিন্তু এইভাবে ছোট একটা ইটের জমাখরচ দেবোত্তরের খাতায় লুকিয়ে বসে আছে তা অনুমান করতে পারেনি।
সম্পত্তির জন্য আমি খাতা ঘাঁটছিলাম না। ঘাঁটছিলাম ওই ঠাকুরদাস পালের খুনের অন্তরালে কোন অনুমানটি সত্য তাই আবিষ্কারের জন্য। ওই সামান্য কি বলেছিলেন ঠাকুরদাস পাল তার জন্য রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর তাঁকে খুন করালেন? রত্নেশ্বর রায়ের পাপপুণ্যে আমার কিছুই করবার নেই। ওর ভাগ বা উত্তরাধিকার নেই। উত্তরাধিকার থাকে বিষয়ের। তা আমি পেয়েছি। কিন্তু এ যে তাঁর পাপ, যদি এটা সত্য হয়, তার পাপই হয়, তবে সেই পাপ যে প্রচ্ছন্ন কলির মত ছুরি বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে তোমার এবং আমার মধ্যের বন্ধনটা কাটবার জন্যে। এ নিয়ে মনে মনে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলেছি। তুমি যেন কেঁদেছ। মুখ ফিরিয়ে বসেছ। তারপর বলেছ—এর পর আর হয় না তোমার সঙ্গে আমার বন্ধন। আমিও ভাবছি, ঠাকুরদাস পাল এমন কোন্ মর্মান্তিক কথা বলেছিল? সে কথা তিনি বলার পরই কি আমিই পারব তোমার সঙ্গে জীবন বাঁধতে? আমি পাগলের মত কাগজ ঘাঁটছিলাম। দেবতার ঘরের সিন্দুকের ভিতর থেকে কাপড়ের টুকরোয় বাঁধা অনেক চিঠি পেয়েছিলাম সোমেশ্বর রায়ের আমলের। বহু বিচিত্র চিঠি। কাত্যায়নী দেবীর আরও ক’খানা সেই ধরনের প্রেমপত্র ছিল, ল্যান্ড-হোল্ডারস অ্যাসোসিয়েশনের চিঠি, রেগুলেশনের নকল পেলাম। নানান জমিদারের চিঠি পেলাম। আর পেলাম রবিনসন নীলকুঠীর কুঠীয়ালসাহেবের একটি চিঠি। তার মধ্যে দেখলাম তিনি তাকে টাকা ধার দিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন না, রবিনসনের ব্যবসায়ে জমিদার হিসেবে সাহায্য করেছেন প্রজাদের নীল বুনতে বাধ্য ক’রে, এবং আরও অনেক কিছু ক’রে। একখানা চিঠি ছিল বীরেশ্বর রায় সম্পর্কে। রবিনসন লিখেছে—“মিস্টার রায়বাবু, তোমার ছেলে ধীরা এখানে বেশী থাকছে বলে তুমি মনে মনে ভয় পেয়েছ শুনলাম। রেভারেন্ড হিল আমাকে বলেছেন। চিন্তা করো না। সে আমাদের ভালবাসে, আমার ছেলে জনি এবং মেয়ে মেরীর সঙ্গে তার খুব ভাব। আমরা তাকে ভালবাসি। দুর্দান্ত সাহসী ছেলে। তবে আমরা তাকে মুর্গী বীফ হ্যাম খাওয়াইয়া ক্রীশ্চান কখনই করিব না। মেরী ইংরেজ মেয়ে; সুতরাং চিন্তা করো না।”
বীরেশ্বর তখন ষোল বছরের।
আরও চিঠি পেয়েছিলাম—একখানা প্রিন্স দ্বারকানাথের। তিনি জানতে চেয়েছিলেন জমিদারী সম্পর্কে কতকগুলো তথ্য। সোমেশ্বর গ্রামে এসে শুধু জমিদারীর খাজনার সঙ্গেই নয় মাটির সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েছিলেন বলে এসব তথ্য তাঁর নখদর্পণে ছিল।
আর একখানা চিঠিতে বর্ধমানের জাল প্রতাপচাঁদের কথা ছিল। দ্বারকানাথ লিখেছিলেন- “শ্মশান হইতে পলায়ন করিয়াছে, মরাটা ভান, ইহা প্রায় আরব্য উপন্যাসের সিন্দুক ওড়ার মতই অবিশ্বাস্য। যাহা হউক সঠিক সকল ঘটনা না জানিয়া ইহাকে আমি সমর্থন অসমর্থন কিছু করিতেছি না। অগ্রে জানিয়া যাহা সিদ্ধান্ত করিব, তদনুসারে কর্ম করিব। পরে এ বিষয়ে আপনাকে সমুদয় জ্ঞাত করাইব।”
আর একখানা পত্রে ছিল-”আপনি গ্রামে বসিয়া পৌত্তলিকতা এবং তন্ত্রমন্ত্র ইত্যাদি বিকৃত আচার লইয়া আছেন ইহাতে আমার দুঃখ হয়। আপনি কলিকাতায় আসুন। মাননীয় শ্রীরামমোহন রায় মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করুন। আমি নিশ্চিত বলিতে পারি আপনার মতের পরিবর্তন হইবে। তাহা ছাড়া অর্থ লইয়া জমিদারী কেনায় আমাদিগকে ভুলাইয়া ইংরাজেরা ব্যবসা-বাণিজ্য সব হস্তগত করিয়া লইতেছে। বাণিজ্যই লক্ষ্মী। সুতরাং আমাদিগকে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও অগ্রসর হইতে হইবে।”
এসব যখন পড়ছিলাম তখন মনের মধ্যে সেকালটা ভেসে উঠেছিল কিন্তু সে আমলের ইতিহাসকে জানার প্রলোভন আমার ছিল না।
আমি জানতে চাচ্ছিলাম ওই ঠাকুরদাস পাল আর রত্নেশ্বর রায়ের কথা। তাতেই আমি এমন মগ্ন হয়ে গেছি যে, শুধু অতীতই বা কেন, বর্তমান কালের আর কিছু মনে ছিল না আমার। কলকাতা, তুমি—সব অনেক দূরে চলে যাচ্ছে যেন। আমি ১৯৩৬ সালের এপ্রিলের শেষে কীর্তিহাটে চোখ মেলে বহুবল্লভ পালের উকীল ছেলে, হাকিম হরেন ঘোষ, রায়বংশের ভাঙা কুঁজোদেহ ধনেশ্বর-কাকা, শিবু পণ্ডিতের আধুনিক সাহিত্যের আলোচনা, সুরেন দের কাছে সেকালের ছ আনা আট আনা মণ ধানের দামের কথা, উরু ভটচাজের মুখে দানীবাবু গিরিশবাবুর বক্তৃতার কথা শুনতে শুনতেও রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের আমলে বাস করছি, আর তাঁকেই জেরা করছি। বলুন—কি হয়েছিল বলুন।
এদিকে ওইদিনের ওই ঘটনার পর গ্রামটা গোটা যেন ছুটে আমার কাছে এগিয়ে এল। সে এক বিস্ময়কর ঘটনা মনে হল আমার। তিন চার বার এসেছি, বাবার শ্রাদ্ধে ক্রিয়াকর্মের সময় সকলকে মিষ্ট ভাষায় সবিনয় সম্ভাষণ করেছি, তারাও মিষ্ট কথা বলেছে, তুষ্ট হয়েছে বলে হেসেছে, কিন্তু তবু কাছে আসেনি। যা হয়েছে দুরে দুরে দাঁড়িয়েই হয়েছে। কিন্তু চারদিন আগের ঘটনাটির ফলে এমন একটা কিছু হয়ে গেল যাতে তারা একেবারে ঠেলে এসে ঘরে ঢুকে চেপে বসল। হেসে বলল -এলাম আমরা।
শুধু ভদ্রজনেই নয়; গ্রামের যাদের আমরা ব্রাত্য বলি তাদের দল এল নালিশ নিয়ে, বললে—আমাদের এইটে বিচার করে দ্যান।
বেশ মদ্যপান ক’রে আবেগবিভোর হয়ে এসে হাজির হল, বললে—লইলে আমরা আর কার কাছে যাব আজ্ঞে? বলে দ্যান!
ওদের প্রথম মামলা নিয়ে মনে হল খুনের মামলার রায় দিতে হবে। সে এক স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ। বুড়ো হাটু বাউড়ী একটি যুবতী মেয়েকে সাঙা করেছিল। যুবতীটি ঘর করতে করতে একটি নব যুবকের সঙ্গে প্রেম করে। তা নিয়ে পাড়ায় হাঙ্গামা অনেক হয়। মারধরও হয়। অবশ্য মেয়েটাকে। এবং ছোঁড়াটাকে কানও মলতে হয়, কিন্তু শেষে মেয়েটা এর সর্বস্ব হরণ করে ছোঁড়াটাকে নিয়ে পাশের গাঁয়ে পালিয়ে গেছে। সেও কীর্তিহাটের সামিল আমাদেরই জমিদারী। মেয়েটা মরিয়া হয়ে আমার সামনেই ঘোমটা খুলে বললে-আমি যাব নি। খাব নি, উর ভাত খাব নি। বুড়ো মড়ার গায়ের গন্ধে আমার ঘুম হয় না!
আমি বিচার করে দিলাম—মেয়েটা যা টাকা গয়না বাসন নিয়ে এসেছে তা ফেরত দিতে হবে। আর ও ওই যাকে বরণ করেছে তার কাছেই থাকবে।
সাধুবাদ পড়ে গিয়েছিল। মেনে নিয়েছিল তারা।
এমনি আর একটা নালিশ সেদিন এসেছিল, গোয়ানপাড়ার নালিশ। মেয়েরা ছিল না। ছিল পুরুষরা। নালিশটা এই—হুজুর মালেক, তোমার জমিনে হামি লোক বাস করি। লেকিন সিটিলমেন্টে গির্জের মালিক কেনো হলদি বুড়ী হোবে। যে মুখপাত্র হয়ে এসেছিল সে নতুন লোক, তাকে দেখি নি। তাকে দেখে মনে হয় না সে মানুষ অন্ততঃ গোয়ানপাড়ার মানুষ! সে যেন এক গল্পলোক বা স্বপ্নলোকের মানুষ। লোকটার দিকে চেয়ে ছিলাম। হঠাৎ রায়বাড়ীতে শাঁখ বাজল। উলু পড়ল। কিছু বুঝলাম না। লোকটার দিকেই দৃষ্টি ফেরালাম। এমন সময় কে যেন ছুটে এল, গোয়ানদেরই ছেলে। সাদি ক’রে বহু নিয়ে আইলো বড়কা বাবুর বড়কা ছেলিয়া। বিরজাবাবু। এই মস্ত বহু। বহুত ফেশন খুবসুরত ভি। আর বিরজাবাবু বঢ়িয়া পোশাক পিহিনকে আইলো। বহুৎ বড়া আদমী হইয়াছে। বড়া নোক্রী মিলল উনকে। বাপরে বাপরে ক্যা কায়দা!
ওদের আর নালিশ করা হল না। ছুটে সব একসঙ্গে চলে গেল। এ লোকটাও চলে গেল।
চুপ করে বসে ছিলাম কিন্তু মনটা চঞ্চল এবং ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। বুঝেছিলাম ব্রজেশ্বর ফিরেছেন এতদিন নিরুদ্দেশের পর কোন এক হতভাগিনীর মস্তক ভক্ষণ করে। কিন্তু বড় চাকরী পেয়েছে বড়লোক হয়েছে সেটা খুব মাথায় এল না। কোন ধনবানকে ঠকিয়ে তার একমাত্র কন্যাকে বিয়ে করে অদৃষ্ট ফিরলে বিস্ময়ের কিছু থাকত না। এ চাকরী!
আজ মেজদি পর্যন্ত আসেন নি! মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল। বোধহয় ওই বধুটির জন্য। রঘুকে বললাম- বেহালাটা দে।
বেহালাটা নিয়ে বাজাতে গিয়ে একখানা ফটোর দিকে চোখ পড়ল। পুরনো ফটোগ্রাফ, ফেড হয়ে গেছে। রায়বাহাদুর রায়বাহাদুর হয়েছিলেন ১৮৮২ সালে, সেই সময়ের চোগা চাপকান পাগড়ি পরা ফটো, হাতে সনদ। বলতে ভুলেছি, সেকালের কতকগুলো ফটো কাছারীতে পড়ে ছিল, কাঁচ ভেঙে, ফ্রেম ভেঙে, সেগুলো আমি নিয়ে এসেছিলাম। রায়বাহাদুরকে বললাম—
—তোমার একেবারে মুছে যাওয়া উচিত ছিল।
রঘু এসে ডাকলে—মেজঠাকুরমা আসলেন!
—ডাক এইখানে! নিচে যে ঘরটায় এখন বাইরে লোকজন বসে সেইখানে বসেছিলাম। মেজদি এখানে না-আসা নন। কেউ না থাকলে আসেন।
রঘু বললে—আরও মাইয়াছেলিয়া আছে।
—আরও মেয়েছেলে?
—নতুন বহু লিয়ে আসছেন।
—অ। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেই উঠে গেলাম।
মেজদি আমাকে দেখেই বললেন—দেখ ভাই নাতি, ব্রজ কেমন বউ এনেছে। তুই এইবার বিয়ে কর ভাই। নাতবউ, এই হল সুরেশ্বর, তোমার দেওর। আর আমার চুলের কালো রঙ। মুখের যদি। অন্নদাতা। রায়বাড়ীর পঞ্চপিদীমের ঘিয়ের পিদীম।
আমি অবাক হয়ে গেলাম সুলতা! চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এ কি বউ! এ যে পরমাসুন্দরী মেয়ে।
বউটিও অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। সঙ্গে রায়বাড়ীর গণ্ডা দেড়েক আইবুড়ো মেয়ে। দেখতে তারা সুন্দরী। বিয়ের বয়স চারটের বয়ে যাচ্ছে। তারা নতুন বিয়ে এবং নতুন বউয়ের রসে মগ্ন। গা-টেপাটেপি করে হেসে যাচ্ছে।
আমি বললাম—নমস্কার!
মেয়েটিও বললে—নমস্কার।
বললাম—বসুন! তোরা বসরে। মেজদি, এদের সব জলটল খেতে দাও!
আইবুড়ো মেয়েদের মধ্যে সব থেকে বড় জগদীশ্বর-কাকার মেয়ে অর্চনা, সে বললে—জল তো শুধু খাব না। তোমার বাজনা শুনব। ব্রজদা বললে, বউ গান জানে। তুমি বাজাও, বউ গান করবে।
অবাক লাগল, প্রমত্ত নটরাজ জগদীশ্বর-কাকার মেয়েটি এমন!
মেজদি বললে-আর তুই নাচবি!
—সে আমি কেন? তুমি নাচবে!
—কেন লা। আমি নাচব কেন? বিয়ে বিয়ে ক’রে ক্ষেপেছিস দাদার সামনে ধেই ধেই করে নাচ। দাদা তাহ’লে বিয়ে দিয়ে দেবে। গতি হবে একটা!
এরই মধ্যে ডাক শোনা গেল—ভাই রাজাবাহাদুর। কই, কোথায়? ওরে বাপরে! করেছ কি তুমি রাজা, এ যে সত্যি সত্যি মহারাজা হয়ে বসে গেছে ভাইয়া।
এসে হাজির হল ব্রজেশ্বর। সেই হাসিমুখ, একটুকু অপ্রতিভতার চিহ্ন নেই। পরনে স্যুট। চমৎকার চেহারা হয়েছে। দেহের শীর্ণতা আর নেই। এসেই হাতখানা চেপে ধরলে। আমি স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। একটু একটু করে সে বিবর্ণ হতে লাগল। হঠাৎ আমাকে টেনে বললে—একটু তাড়াতাড়ি আছে ভাই। পরে আসব। একটা কথা বলে যাই।
ব্রজেশ্বরের হাত ধরে আমিই টানলাম। বললাম- মেজদি, তুমি এদের খাওয়াও। আমি ব্রজদার সঙ্গে কথা বলি।
ওকে টেনে একেবারে নিরিবিলি ঘরে নিয়ে গিয়ে বললাম—কি ব্যাপার?
হেসে বললে—অনেক ব্যাপার রাজা। শেফালির ব্যাপারটার জন্যে তোমার কাছে আমার অনেক লজ্জা। মাফি মাংছি ভাই। মাফি কিয়া যায় রাজা! উ ভাই হামার কসুর হুয়া। স্রেফ নেশার ঝোঁকে বলে ফেললাম আমি সুরেশ্বর রায়। ট্যাক্সিতে চাপিয়ে জানবাজারের বাড়ীর কাছে গাড়ী দাঁড় করিয়ে, বাড়ীর দরজায় আজেবাজে কথা বলে ওদের কাছে খাতিরটা জমিয়েছিলাম ব্রাদার। ঝোঁকে পড়ে গেলাম। জ্ঞান ছিল না। হিহি করে হেসে বললে—জ্ঞান কোনকালে নেই। করি কি বল! রায়বাড়ীর নামটা আর ওই দালানটা ছেলেবেলা থেকে মাথা খেয়েছে। শেফালিকে বললাম বাঁধা রাখব। বাড়ী ভাড়া করলাম। টাকা তুমি একশো টাকা দিয়েছিলে, আর মাড়োয়ারীর বাড়ী হচ্ছিল, লোহার কড়ি ছিল, তাই দুখানা বেচে টাকা প্রথমটা জুগিয়েছিলাম। ইটও কিছু বেচেছিলাম। শেষে দেখলাম ধরা পড়ব। ভেগে গেলাম রাজা। তোমার কাছে আসতে সাহস হল না, লজ্জাও হল। শেষ বুদ্ধি মাথায় খেলল। ঘুরছি চৌরঙ্গী ধরে। তোমার বাড়ী যাব বলে যেতে না পেরে দক্ষিণমুখো হাঁটা দিয়েছি। কাবলী ছোলাভাজা পকেটে, চিবুচ্ছি। হঠাৎ দেখলাম মহারাজা অজিতেশ্বর প্রসাদের বন্ধ ফটকটা খোলা, দরজা দিয়ে তিনখানা মোটর বেরিয়ে গেল। ফটকের সেন্ট্রিটা খট ক’রে পা ঠুকে সেলাম করলে। বুঝলাম রাজাসাহেব এসেছেন—ওঃ মনে হল, শা—লা, রাজা যদি একটা হতাম এমনি। গাছতলায় বসে থাকতে থাকতে ফন্দি এল মাথায়। মাথায় ধুলো মাখলাম, কাপড়টা খানিকটা ছিঁড়লাম। জামাটার পকেটটা ছিঁড়লাম। বসেই রইলাম, পথের দিকে তাকিয়ে। এক সময় দেখলাম রাজার গাড়ী ফিরছে। গিয়ে ফটকের সামনে দাঁড়ালাম। গাড়ী ভেতরে ঢুকল। আমি হেঁট হয়ে নমস্কার করলাম। গাড়ী ঢুকে গেল। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। সে বিকেল পর্যন্ত। আবার গাড়ী বের হল। ফের নমস্কার। গাড়ী চলে গেল। সন্ধ্যের সময় ফিরল। তখনও দাঁড়িয়ে, তখনও নমস্কার। দাও ভাই, তোমার ভাল সিগারেট দাও।
আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম। সিগারেট ধরিয়ে ব্রজেশ্বর বললে, এ ফন্দি আমাকে সুখেশ্বরকাকা শিখিয়েছিল। মধ্যে মধ্যে পত্র লিখত বড় বড় রাজাকে। লিখত- আমি রাজবংশের ছেলে আজ নিঃস্ব, চাকরী করতে পারি না, লেখাপড়া শিখিনি। বড় দুঃখে আছি। সাধারণের কাছে হাত পাততে পারি নে। একটা সংস্কৃত শ্লোক লিখত, “যাচনা মোঘা বরম অখি গুনে নাধমে লব্ধকামাঃ।” টাকা আসত কিছু কিছু। সেই ফন্দি মাথায় গজিয়েছিল। যাক, সন্ধ্যের সময় বারবার তিনবার আমাকে দেখে রাজাসাহেব জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন, কি চাই? বললাম —কাগজ দাও লিখে দি। লিখে দিলাম—“প্রিন্স অব কীর্টিহাট স্টেট, ওয়ান্টস টু টেল হিজ পেথেটিক স্টোরি।”
বাস, ডাক এল। গেলাম। ওই বললাম—আমি কীর্তিহাটের প্রিন্স, আমরা সিন্স দি টাইম অব আকবর শাহ প্রিন্স। ইংরেজ টাইমে আমাদের উপর অনেক অত্যাচার হয়েছে। আজ গরীব। কিন্তু ইওয়োর হাইনেস, শান্তিপুরের ধুতি ছাড়া পরতে পারি না, সিল্কের জামা ছাড়া গায়ে দিতে পারি না। স্কিন ছড়ে যায়। আজ আপনি যদি সাহায্য না করেন তবে মরে যাব।
রাজা বললেন, তোমার চেহারা দেখে বুঝতে পারছি তুমি ঝুটা বাত বলে নি। কিন্তু কিছু টাকায় তোমার কি হবে? চাকরী কর। বললাম—ইওয়োর হাইনেস, লেখাপড়া জানি না। বাধা দিয়ে রাজা বললেন, কিছু দরকার নেই, তোমার সহবৎ আছে, ইউ নো ম্যানারস। তুমি আমি আমার ছেলের একজন এডিকং হয়ে থাকবে। মাইনে পাবে। তুমি বিয়ে করেছ? বুঝলাম বিয়ে হওয়া-না-হওয়ার উপর মাইনে নির্ভর করছে। বললাম, করেছি। মাইনে হল দেড়শো টাকা। ফ্রি কোয়ার্টার। এবং পোশাক সুট তাছাড়া চুস্ত পাজামা শেরওয়ানী তাও পাব।
চলে গেলাম সেখানে। মাস কয়েক পর রাজা ধরলেন, ক্যা মতলব? তুমি বহু আনো না, রূপেয়া ভেজো না। ক্যা মতলব? বললাম —হুজুর, বউ শ্বশুরবাড়িতে আছে, যাব আর নিয়ে আসব।
ভেবেছিলাম রাজা, পালিয়ে এসে আর যাব না। মানে বউ কোথা পাব? কলকাতায় এসে কিন্তু বউ পেয়ে গেলাম। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে। এক নারীকল্যাণ আশ্রমের পাণ্ডার সঙ্গে। চাঁদা তুলে আশ্রম চালায়, বড় বড় ধনী লোকে চাঁদা দেয়। অন্যথা বিধবা কলঙ্কিনী কুমারী এইসব মেয়েদের আশ্রয় দেয়। খেতে পরতে দেয়। বিয়ে দিয়ে দেয়। আবার পেট্রনদের মনোরঞ্জনের জন্যেও এদের কাজে লাগায়। মেয়েগুলো বলতে গেলে কয়েদীর মত থাকে। দু-চারটে ভাল আশ্রম আছে। সে বললে—তার জন্যে ভাবনা কি। বউ দিতে পারি। এস। তুমি বন্ধু লোক। একটি মেয়ে আছে বুঝেছ, খুব সুন্দরী, বয়স একটু হয়েছে, বিধবা দেওর অত্যাচার করেছিল। মেয়েটা চীৎকার করে লোক জানাজানি করে। কেসে দেওরের কনভিকশন হয়ে গেছে। কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে স্থানও গেছে। কোর্ট থেকেই নিয়ে এসেছি। কিন্তু নানা ঝঞ্ঝাটি ওকে নিয়ে। বিদেয় করতে চাই। দেখ, বিয়ে দিতে পারি। দেখলাম, বয়স আমার সমান হবে হয়তো। তাতে আমার কিছু যায় আসে না। বিয়ে করে ফেলেছি। ওখানে নিয়ে যাবার সময় সব বলেছিলাম। সরমা ভাল মেয়ে। কিন্তু ওর সন্দেহ এখনও আছে আমি ফেলে পালাব। তাই এবার কুমারবাহাদুরের কাজে কলকাতা এসেছি, কুকুর কিনতে হবে। একজোড়া ফার্স্ট ক্লাস অ্যালসেসিয়ান চাই। আমার উপর ভার পড়ল। ও আমার সঙ্গ ছাড়ল না। বললে—সঙ্গে যাব আমি। আর ছুটি নাও, তোমার দেশে গিয়ে তোমার বাবা-মাকে প্রণাম করে আসব। ভাল লাগল। মনে একটা বাসনাও ছিল একবার সেজেগুজে কীর্তিহাটে আসব। আমার এখানকার পজিশনটা দেখাব। বেশী দেখাবার ইচ্ছে ছিল সুখেশ্বর কাকাকে। জান রাজা, এই লোকটিকে মেরে আমার ভাইটা পাগলা গারদে গেছে তাতে আমার একবিন্দু দুঃখ নেই। আমার বাবা মাতাল বজ্জাত গোঁয়ার সব। কিন্তু সুখেশ্বর-কাকা ছিল স্নেক —পাইথন অজগর! বাবারে বাপরে! তা সে নেই কিন্তু তার ছেলেরা আছে। তারা দেখুক। এখানে এসে শুনলাম তুমি আছ রাজা। আর যা করেছ না তা রাজার মতই করেছ। লোকে ধন্য ধন্য করছে।
সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বললে-দেখো, আমি লেখাপড়া শিখিনি, আমার অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়েছে, মিথ্যে বলি হরদম, তোমার অনেক আছে, তোমাকে হিংসেও করতাম। তা এখনও করি। মাঝে মাঝে করি। সব সময় করি না। বিলিভ মি। আবার ভালও বাসি। আমি শেফালি ওখানেও গিয়েছিলাম। এবার না। এর আগের বার কুমারসাহেবের সঙ্গে চারদিনের জন্য এসেছিলাম। সেই সময়। শেফালি খ্যাংড়া নিয়ে তেড়ে এল। আমাকে তো জান। আমি মানাতে জানি। বললাম, তাই মারো। পিঠ পেতে দিচ্ছি। তারপর বসে একটু পান টান করে কিছু টাকা দিয়ে বললাম- দেখো আমি যাই হই বেইমান নই। না হলে আসতাম না। আর বড়বংশের ছেলেও বটে। তখন ও তোমার কথা বললে। বললে, হ্যাঁ এই একটা মানুষ বটে! বললে সব কথা। আমি রাজাভাই, পাপী মানুষ, আমি ব্রজেশ্বর, কিছুদিনের মধ্যেই ওখানে ঘুন হয়েছিলাম। সন্দেহ হল কোনখানে নিশ্চয় ঢুকেছ। পথে ঘুরে বেড়িয়েই তো প্রথম সাহস সঞ্চয় হয়। প্রথম কলকাতায় গিয়ে চীৎপুরের ট্রামে ঘুরতাম। সন্ধ্যে থেকে দশটা পর্যন্ত। তারপর পায়ে হেঁটে। তারপর সুড়সুড় করে মুড়ি দিয়ে ঢুকলাম। তারপর হাঁক ডাক মেরে। কিন্তু দেখলাম রাজার ছেলে এসেছিল দুঃখীর দুঃখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, রাজার ছেলের মতই ফিরে গেছে। ঢোকে নি কোথাও। সেলাম দিলাম। কুর্নিশ
আমি অবাক হয়ে শুনলাম। বিচিত্র চরিত্র এই মিষ্টমধুর পাষণ্ডটিকে কি বলব খুঁজে পেলাম না।