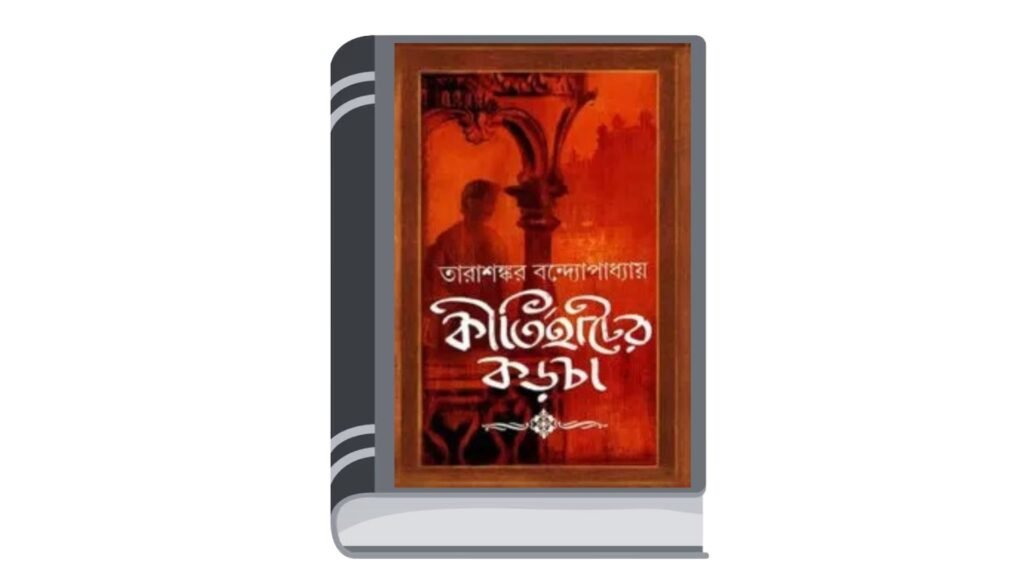কীর্তিহাটের কড়চা – ৪.৯
৯
পাগল একদৃষ্টে ছবির দিকে তাকিয়েছিল। বীরেশ্বর রায় অধীরভাবে অপেক্ষা করছিলেন পাগলের কথার জন্য।
কি বলবে পাগল? পাগলের কথাগুলো তাঁর মনের মধ্যে যেন চারিপাশ থেকে প্রতিধ্বনি তুলছে; সর্বনাশী, ছলনাময়ী—মোহিনীরূপে ভয়ঙ্করীও।
কি অর্থ তার, তাই তিনি শুনতে চান।
ছবিখানা প্রকাণ্ড বড়। ভবানীর পূর্ণাবয়ব মূর্তি। একখানা চেয়ার ধরে সে দাঁড়িয়ে আছে রাজরাণীর মত। বীরেশ্বর রায় তাকে রাণীর মতো সাজিয়ে নিয়ে আসতেন ওই সামনের বারান্দায়; চেয়ারের হাতল ধরে ভবানী দাঁড়াত, তিনি দুরে বসে থাকতেন; আর সাহেব-পেন্টার ছবি আঁকত। এক পোশাক, এক গহনা, একরকম চুলের বিন্যাস। ভবানীর চুল ছিল, আশ্চর্য চুল। প্রায় তার হাঁটু ছুঁইছুই করত। আর পরিমাণেও ছিল প্রচুর। সাহেব যেদিন ছবি আঁকত, সেদিন সাহেবের নির্দেশমত তাকে মাথা ঘষতে হত। চুলের রাশি ফুলে ফেঁপে উঠত, কালো মেঘের পুঞ্জের মত। ভবানীর রঙ ছিল শ্যামবর্ণ। নাকে ছিল একটা বেশ বড় দামী হীরের নাকচাবি। জ্বলজ্বল করত সেটা। চিত্রকরসাহেব অবিকল তাকে ফুটিয়ে তুলেছে ছবিতে। অবিকল। বীরেশ্বর রায়ের মধ্যে মধ্যে রাত্রে নেশার ঝোঁকে তাকে জীবন্ত বলে ভ্রম হয়। তাকে তিরস্কার করেন। কিন্তু তাকে পাগল চিনলে কি করে? তাঁর ধারণা হয়েছে ভবানীকে পাগল দেখেছে, ভবানী ঘর থেকে চলে যাওয়ার পর। না হলে চেনা অসম্ভব। অসম্ভব।
ভ্রূ কুঞ্চিত করে অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছিলেন রায়।
পাগল একটু এগিয়ে গেল। চেয়ারের হাতলে রাখা হাতখানার উপর ঝুঁকে কি দেখছে। ছ’টা আঙুল ছিল ভবানীর। ডান হাতে, কড়ে আঙুলের পাশে ছোট্ট একটা আঙুল ছিল। সেটি পর্যন্ত স্পষ্ট করে আঁকতে চিত্রকর ভোলেনি।
পাগল আঙুলটির উপর হাত দিলে এবং প্রশ্ন করলে-ছ’টা আঙুল? এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়। ছ’টা!
রায় বললেন—হ্যাঁ, ওর ছ’টা আঙুল ছিল।
পাগল আবার ছবির মুখের দিকে তাকালে। তারপর বললে—ওটা? আঙুল দিলে সে ছবির সিঁথির কাছে। একটা ঘূর্ণি—বাহার নয়?
—হ্যাঁ। ওর কপালের মাঝখানে চুলের সিঁথির মুখে চুলের একটা ঘুর্ণি ছিল!
—হুঁ। চোখের চাউনি? সে-চাউনি তো নয়। উঁহু। পাগল শুধু ঘাড় নাড়তে লাগল। না-না-না! না!
—কি?
—সে তো নয়! এ সে তো নয়! তবে—
—কি তবে?
—তবে তো এ-এ-এ—
–কি? এ কে?
পাগল অকস্মাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ওঃ-ওঃ-ওঃ।
রায় বললেন—বল, এ কে? তুমি চেন?
পাগল ঘাড় নাড়তে লাগল-না-না-না।
অকস্মাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন বীরেশ্বর রায়। মশালটা দুরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দুই হাতের সবল থাবার দুই কাঁধ ধরে নিষ্ঠুর ঝাঁকি দিয়ে বললেন—বল। বল। কোথায় দেখেছ ওকে? কোথায় থাকে ও?
পাগল তাতে বিচলিত হল না, সে বারেকের জন্যও ফিরে তাকালে না বীরেশ্বরের দিকে অর্থাৎ প্রশ্নও জাগল না তার মনে, কেন এমন রূঢ়ভাবে প্রশ্ন করছে সে। ছবির দিকে তাকিয়েই রইল। এবং সেই ঘাড় নেড়ে বলতে লাগল—না-না-না। এ নয়, এ নয়। তার ছ’টা আঙুল ছিল না। তবে ট্যারা ছিল। এ কম, সে বেশী। এ তো সে নয়।
বীরেশ্বর বুঝতে পারলেন না কথার অর্থ। ভ্রূ কুঞ্চিত করে একটু বুঝতে চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন—সে কে?
—সে? ওই ছবির দিকে তাকিয়ে থেকেই সে উত্তর দিলে।
—হ্যাঁ, সে কে?
—সে মায়াবিনী, সে–সে ডাকিনী।
—ডাকিনী?
—হ্যাঁ। হ্যাঁ। কামাখ্যা মন্দিরে সে ডাকিনী! এ সে নয়। না। ছ’টা আঙুল তার ছিল না। এ একটু ট্যারা, সে অনেক ট্যারা ছিল। নইলে অবিকল সেই।
এবার রায়ের দিকে ফিরে বললে-ও কে? তুমি এ-ছবি কি করে পেলে? ওর-ওর নাম কি? মহালক্ষ্মী?
—না। ভবানী!
—ভবানী? ভবানী? হ্যাঁ। ঠিক, ঠিক! ও কোথা? হ্যাঁগো! ও কোথা?
—জানি না। তোমার কাছে জানতে চাচ্ছি—তুমি তো লোকে বলে সিদ্ধপুরুষ—বলতে পার, ও কোথায়?
—না-না-না। আমি কিছুই নই। ওই—ওই গন্ধ আনতে পারি। ওই ধুলো গুড় করতে পারি। ওই দিয়েই সে-মায়াবিনী সব কেড়ে নিয়ে গেল। তার ভয়ে আমি পালিয়ে বেড়াই।—
বলতে বলতে সে আবার নিজের গলা টিপে ধরলে। এমন জোরে সে টিপে ধরলে যে, চোখদুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে বলে মনে হল। একটা বিকৃত গোঙানি তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করলে।
রায় আবার তার হাত চেপে ধরে টেনে ছাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু আশ্চর্য। তার হাতের মুঠো লোহার সাঁড়াশির মত শক্ত হয়ে উঠেছে। তবুও রায় তার থেকে অনেক বলশালী। ছাড়িয়ে দিলেন। লোকটা অবসন্ন হয়ে পড়ে গেল মেঝের উপর। মেঝের উপর পড়ে সে কাঁদতে লাগল।
কিছুক্ষণ পর বীরেশ্বর তাকে একটা ঘরে ঢুকিয়ে বললেন—এই ঘরে তুমি থাকবে। আমি বাইরে থেকে তালা দেব। কাল সকালে খুলে দেব। তোমাকে কাল সকালে যেতে হবে সোফিয়া বাঈজীর বাড়ী। তাকে তুমি কি করেছ? সে প্রলাপ বকছে। তোমার কাছে মাফ চাচ্ছে। তাকে ভাল করে দিতে হবে তোমাকে।
পাগল কথা বললে না, মেঝের উপর লুটিয়ে শুয়ে পড়ল। রায় বললেন—ওই তো খাটে বিছানা করা রয়েছে, উঠে শোও।
সে উত্তর দিল না। পড়েই রইল।
—শুনছ।
পাগল তবু সাড়া দিল না। রায় বিরক্তিভরে দরজা বন্ধ করে দিয়ে চাকরকে বললেন—তালা নিয়ে আয়।
চাকর তালা নিয়ে এল, তিনি নিজে হাতে তালা দিয়ে চাবিটা নিয়ে নিজের কাছে রাখলেন।
.
সকালবেলা, তখন প্রায় সাড়ে ন’টা, তখন ঘুম ভাঙল বীরেশ্বর রায়ের। উঠে চাকরকে ডাকলেন। চাকর বাইরে দাঁড়িয়েই ছিল এই ডাকের প্রতীক্ষায়। সে ভিতরে গিয়ে দাঁড়াল। বললে-ও-ঘরে—
—কি ও-ঘরে—
—ওই সেই পাগলাবাবাকে তালা দিয়ে রেখেছেন—
—হ্যাঁ। কি? সে নেই?
—আজ্ঞে না। খুব গোঙাচ্ছে। আর খুব দুর্গন্ধ উঠছে।
—গোঙাচ্ছে? দুর্গন্ধ উঠছে?
—খুব!
—দরজা ফাঁক করে দেখেছিস? কি ব্যাপার? দেখিসনি?
–আজ্ঞে না। ভয়ে কেউ ওদিকে যাইনি আমরা।
রায় চাবিটা তার হাতে দিয়ে বললেন—যা, খুলে দেখ।
সে চাবি হাতে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। অর্থাৎ তার ভয় করছে।
—আচ্ছা আমি মুখ-হাত ধুয়ে যাচ্ছি।
তিনি উঠে গোসলখানায় ঢুকলেন। গোসলখানা থেকে বেরিয়ে এসে তিনি বারান্দার ওপাশে বদ্ধ ঘরটার দরজায় দাঁড়িয়ে চাকরের কথার সত্যতা বুঝতে পারলেন। একটা জন্তুর মতো গোঙানি উঠছে আর দুর্গন্ধে যেন বমি আসছে। তিনি নাকে রুমাল বাঁধলেন। তারপর তালা খুলে দরজা দু’পাট ঠেলে খুলে দিলেন।
দেখলেন সে এক বীভৎস দৃশ্য।
লোকটা ঘরময় মলমূত্র ত্যাগ করে তারই উপর পড়ে আছে; সর্বাঙ্গে যেন মেখেছে, মুখে পর্যন্ত লেগেছে। মনে হল মুখ রগড়েছে ময়লার উপর। তার উপর লোকটা জ্ঞানশূন্য, দেখেই বোঝা যাচ্ছে অসুস্থ। গলা দিয়ে নিষ্ঠুর যন্ত্রণাকাতর একটা শব্দ গোঙানির মত বের হচ্ছে।
থমকে দাঁড়ালেন বীরেশ্বর। এ কি বিপদ! এ কে পরিষ্কার করবে? একটু চুপ করে ভেবে নিয়ে বললেন—কি করবে ওকে নিয়ে? এ্যাঁ?
—আজ্ঞে! বলে চাকর চুপ করে রইল। পিছনে বারান্দায় তখন চাকরবাকরেরা অনেক এসে জুটেছে। এমন কি নায়েব কর্মচারীরাও।
—নায়েবাবু? তাহলে মেথর ডাকুন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চাকরেরা শিউরে উঠল।
নায়েব এসে বললে—আজ্ঞে হুজুর উনি সিদ্ধপুরুষ, মেথর দিয়ে—
—তাহলে, লোকটিকে পরিষ্কার করতে তো হবে। অন্তত তুলে নীচে কোথাও নামিয়ে দিতেও হবে। সিদ্ধপুরুষকে ওই ভাবে রাখাও তো ঠিক হবে না!
—আপনি যান হুজুর, যা হয় আমরা করছি। চাকরবাকরেরা শুদ্র বলে ওকে ছুঁতে ভয় করছে। ব্রাহ্মণ যাঁরা আছেন, তাঁরা করবেন। আপনি যান।—
রায় চলে এলেন। গত রাত্রিতে তিনি একরকম মদ্যপান করেনই নি। পাগলকে ঘরে বন্ধ করে গিয়ে কাপড়চোপড় ছেড়ে খাবার আগে ও পরে অতি অল্প পরিমাণে খেয়ে শুয়ে পড়েই ঘুমিয়ে গিয়েছিলেন। লোকটা সম্পর্কে ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে গিয়েছিলেন। গতকাল দিনে তিনি ঘুমোন নি—সারা দুপুর ভেবেছিলেন রাধাকান্ত দেববাহাদুরের কথা। তাঁর সংস্পর্শে এসে প্রথম জীবনে বিবাহের পর যে কয়েক বৎসর শান্ত-সংযত জীবনযাপন করেছিলেন তখনকার কল্পনার কথা মনে পড়েছিল। আর মাঝে মাঝে ভেবেছিলেন, সোফিয়ার কথা এবং এই পাগলের কথা। সন্ধ্যার মুখে সোফিয়ার বাড়ি গিয়ে তার অবস্থা দেখে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত ওই পাগলকে খুঁজেছেন। বাড়ি এসে বাড়ির দরজায় পাগলকে পেয়ে তাকে নিয়ে ঘণ্টাদেড়েক তার সঙ্গে কাটিয়ে তার অসংবদ্ধ প্ৰলাপ থেকে এইটুকু বুঝেছিলেন যে, পাগল ভবানীকে দেখেনি। অর্থাৎ তার মুখে সে জীবিত আছে এ-সংবাদ পাননি। তাতে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন, খানিকটা ক্লান্তি এবং নিশ্চিত্ততার মধ্যে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এবং মদ বেশী পরিমাণে খেয়ে জ্ঞান হারাতেও ঠিক ভাল লাগেনি!
ঘরে এসে বসতে চাকর এসে দাঁড়াল। বললে-বেরেকফাস্টো দেয়া হয়েছে হুজুর।
রায় তখন বিলিতীকেতায় সকালে খেতেন ব্রেকফাস্ট। টেবিল ছিল, চেয়ার ছিল দস্তুরমত। কফি, রুটি-মাখন, ডিম, কেক দিয়ে ব্রেকফাস্ট। দুপুরে দেশীমতে ভোজন, রাত্রে বিলিতী নয়, একেবারে নবাবী আমলের পোলাও-কালিয়া-কোর্মা। ভবানীর অন্তর্ধানের পর এই ব্যবস্থা। তবে মদটা সব সময়েই থাকত।
রায় চেয়ারে বসে বললেন—মদটা নিয়ে যা।
চাকর বিস্মিত হল।
রায় রুটি-মাখনের পাত্রটা টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন- পাগলকে কে পরিষ্কার করছে?
—আজ্ঞে, খাজাঞ্চীবাবু।
—হরি চক্রবর্তী?
—হ্যাঁ। বলছেন—গায়ে খুব তাপ। পেবল জ্বর।
—হুঁ, তা নইলে বেহুঁশ হবে কেন? পরিষ্কার করে খানিকটা আতর গায়ে মাখিয়ে দিতে বলবি। আর কাউকে বল–বউবাজারে সোফি বাঈয়ের বাড়ী গিয়ে সে কেমন আছে খবর নিয়ে আসবে। দেখ, হয়তো বসীর এসেও থাকতে পারে।
—নায়েববাবু বলে দিলেন, আজ শ্যামবাজারে হুজুরের জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ীতে ছেরাদ্দের নেমন্তন্ন আছে। আপনি যাব বলেছিলেন!
বীরেশ্বর রায়ের মনে পড়ল —হ্যাঁ, আজ জ্যাঠাইমার সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ হবে, তার সঙ্গে সমারোহের সঙ্গে দান-উৎসর্গ হবে, আদ্যশ্রাদ্ধের সময় এসব হয়ে ওঠেনি।
কুড়ারাম রায় ভটচাজের শ্যালক-পুত্র, বাবা সোমেশ্বর রায়ের মামাতো ভাই, হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর জ্যাঠা। এ পর্যন্ত রায়বাড়ীর জ্ঞাতিকুটুম্বের মধ্যে বলতে গেলে ওই একমাত্র কুটুম্ববাড়ী। তবুও সে-সম্পর্ক তিনি রাখতে পারেননি। একটা ক্ষত আছে। ওই জীবনের সব থেকে বড় এবং একমাত্র ক্ষত ভবানী। হরিপ্রসাদকাকার ছেলে রমাপ্রসাদের বিয়েতে গিয়েই তিনি ভবানীকে দেখেছিলেন। ভবানীকে নিয়ে যখন কলকাতায় ছিলেন, তখন ও বাড়ীতে যাওয়া-আসা ছিল নিয়মিত। জগদ্ধাত্রী বউদির সঙ্গে ভবানীর সখিত্বও ছিল। ভবানী —। তার চলে যাওয়ার পর তিনিও যাননি ও-বাড়ীতে, ওরাও আসেননি এ-বাড়িতে। ওই একমাত্র সামাজিক ক্রিয়াকর্মে যান। তাঁর বাড়ীতে ক্রিয়াও নেই, কর্মও নেই; না অন্নপ্রাশন, না উপনয়ন, না বিবাহ! একটা কর্ম বাকি আছে। না দুটো। একটা ভবানীর মৃত্যু-সংবাদ পেলে নষ্টশ্রাদ্ধ উদ্ধার করবেন, আর একটা বাকি তাঁর শ্রাদ্ধ, সে কে করবে ভগবান জানেন, কিন্তু তখন তিনি থাকবেন না। তবে তাঁকে আজ যেতে হবে। যাওয়া উচিত। হ্যাঁ, উচিত। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রায় বললেন—হ্যাঁ, যেতে হবে বইকি। কাপড়চোপড় ঠিক কর। হ্যাঁ, যেতে হবে।
সুরেশ্বর বললে—তোমার মনে আছে সুলতা, কালীঘাটের দরিদ্র পরিবারে বিয়ে করেছিলেন কুড়ারাম রায় ভটচাজ। কালীঘাটের হালদাররা সেখানকার সমাজপতি। তাঁদের কাছে এই চাটুজ্জে পরিবার অনেকটা একঘরে ছিল। অভিযোগ ছিল—প্রৌঢ় চাটুজ্জে জাহাজী সাহেবদের খানাপিনার জিনিস-কারবারীদের চাকরি করতেন। পদে ছিলেন সরকার। খানার গোস্ত আসত বড় বড় ঝুড়িতে, মাথায় করে আনত যারা, তারা কোন্ জাত কে জানে, তবে আসত গোমাংস, শুকর-মাংস-বীফ, হ্যাম; জাহাজে সেসব তাঁকে ছুঁতে নাড়তে হত। কিন্তু মাইনে ছিল যৎসামান্য, আর কিছু পাওনা পেতেন কাপ্তেন সাহেবদের কাছে বকশিশ। কিন্তু এতে তাঁর অভাব মেটেনি। তবে চলে যেত কায়ক্লেশে। জাত গিয়েও পেট ভরেনি।
কুড়ারাম রায় ভটচাজমশায় বিয়ের পর শ্বশুরকে চাকরি ছাড়িয়েছিলেন, কাজে লাগিয়ে- ছিলেন নিজের কাছে। আর শ্যালক ছিল একটি—গুরুপ্রসাদ, তাঁকে লাগিয়েছিলেন কোম্পানীর সেরেস্তায় নিজের অধীনে; দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ তাঁর দরখাস্ত মঞ্জুর করেছিলেন। গুরুপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় অর্থোপার্জন করে কালীঘাট ছেড়ে শহর কলকাতায় জোড়াসাঁকো অঞ্চলে বাড়ী করেছিলেন। গুরুপ্রসাদ বেশী দিন বাঁচেন নি। তবে ছেলে হরিপ্রসাদকে ইংরিজী লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। তাঁর গায়ে সেকালে ব্রাহ্মধর্মের বাতাস লেগেছিল। তবে ওদের সঙ্গে সরাসরি জাতে উঠতে তাঁর সাহস ছিল না। হরিপ্রসাদ বীরেশ্বর রায়ের জ্যাঠামশায়। সোমেশ্বর রায় থেকে বয়সে বড়। হরিপ্রসাদের বড় ছেলে দেবপ্রসাদের ডাকনাম নারায়ণচন্দ্র। বয়সে বীরেশ্বর রায় থেকে বড় কিন্তু বন্ধুই। তাঁরই বিয়েতে গিয়ে তিনি ভবানীদেবীকে দেখেছিলেন। তাঁরই মাতৃশ্রাদ্ধ। ব্রাহ্মধর্মের বাতাস গায়ে লাগলেও, মাতৃশ্রাদ্ধে গোঁড়া হিন্দুত্ব বজায় রেখে শ্রাদ্ধ করেছিলেন। অনেক সমারোহও করেছিলেন। আদ্যশ্রাদ্ধ তিলকাঞ্চন করে সেরে রেখে ছ’মাসের মাথায় সমারোহ। একালে হিন্দু যারা, তারাই জানে না তো তোমরা তো ব্রাহ্ম, তোমাদের না-জানারই কথা, তাই বলছি। আমিই কি জানতুম সুলতা? জানতুম না। বাবার মৃত্যুর পর সম্পত্তির জন্যে গোঁড়া হিন্দুমতের একেবারে খুঁটিনাটিটি পর্যন্ত পালন করিয়েছিলেন ঘোষাল ম্যানেজার মায়ের মৃত্যুর পর পালন করিয়েছিলেন মেজঠাকুমা। আদ্যশ্রাদ্ধের সময় কলকাতা এসেছিলেন। তারপর প্রতি মাসে তাঁর পোস্টকার্ড আসত —আঁকাবাঁকা মোটা হরফে লিখতেন, ভাই, বউমায়ের মাসিক শ্রাদ্ধটি করিতে যেন ভুলিবে না। অনেকে এক মাস, দু’ মাস বাদ দিয়া তিন মাস বাদ দিয়া এক মাসে দুটো-তিনটা সারে, সেটা ‘অশাস্তরীয়’ হয় না হয়তো। কিন্তু ভাই, তিন মাস খাইতে না দিয়া এক মাসে তিন মাসের খাওয়া কি মানুষ খাইতে পারে? ওটা যারা করে, তারা নিশ্চয় মাকে ভুলিয়া যায়। তোমার মাকে তুমি ভুলিতে পার না।
শ্রাদ্ধ সম্পর্কে মত জিজ্ঞেস করতে হলে পরলোক সম্বন্ধে মত বলতে হয়। সে-মতামতের কথা থাক। আর মতামতেরই বা মূল্য কি আমাদের, যারা রামের দলে থাকলে রামের কথা বেদবাক্য ভাবি, আবার দল ভেঙে হরির দলে গিয়ে হরির কথা শুধু বেদবাক্যই ভাবিনে রামকে গালিগালাজ করি। আমি কোন দলেরই নই। তবু মেজঠাকুমার কথাটা পালন করেছিলাম অক্ষরে অক্ষরে।
দোহাই তোমার সুলতা, তুমি মুখ খুলবে মনে হচ্ছে, কিন্তু দোহাই খুলো না। তোমাকে আমি ইঙ্গিত করে কিছু বলিনি। আমি শাক্ত নই, শৈব নই, বৈষ্ণব নই, সৌর নই—কংগ্রেস নই, কম্যুনিস্ট নই, আর্টিস্ট হিসেবে প্রগ্রেসিভ নই; রি-অ্যাকশানারী বলতে চাও বলতে পার, তবে আমি তাও নই। কলকাতায় থাকতে বিদগ্ধ কাগজসমূহে ‘সহজিয়া’ কাস্টের কথা পড়েছিলাম—পণ্ডিতব্যক্তিদের কাছে এ সম্পর্কে দুর্বোধ্য আলোচনা শুনেছিলাম, কিন্তু বস্তুটা কি, তার মাথামুণ্ডু কেন—সাকার না নিরাকার, পিণ্ডাকার না তরল পদার্থ—কিছুই ধারণা হয়নি। কীর্তিহাটে গিয়ে বাউলদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, সে পরে বলব, তবে তাদের দেখে বুঝেছিলাম ব্যাপারটা কি! খ্যাপা গোপাল দাসকে একদিন আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সহজিয়াটা কি? সে হেসে বলেছিল—হরি, হরি, হরি-নিজে ওই পথ ধরে বলছ ওই পথটা কি? নেশা করেছ, চোখ ঢুলঢুল করছে, তবু শুধাও নেশাটা কিরকম? বাবাধন, এই যে সহজ পথে, সবার ‘সাঁথে’ পেরেম করে হাটন ধরেছ-এই তো সেই পথ। আমি সেদিন বসেছিলাম ওই কাঁসাইয়ের ওপারে, যেখানটাকে সিদ্ধপীঠ বলে সেইখানে। জমেছিল সেখানে ওই গোয়ানপাড়ার গোয়ানরা থেকে ওপারের কীর্তিহাটের ব্রাত্যরা পর্যন্ত। সকলে চাঁদা করে ভোগ দিয়েছিল মায়ের। খাওয়া-দাওয়া চলছিল। তার মধ্যখানের মধ্যমণি বলব না-মাঝের মানুষ ছিলাম আমি। সভায় যাকে প্রধান অতিথি বলে।
একটু থেমে সুরেশ্বর বললে —তার আগে বীরেশ্বরের কাহিনী থেকে কি করে উনিশশো ছত্রিশ সালে কীর্তিহাটে পরবর্তী পঞ্চমপুরুষ সুরেশ্বর রায়ের জীবনে এলাম, সেটা বলে নিই, বীরেশ্বর রায়েই ফিরে যাই।
***
বীরেশ্বর রায় তাঁর স্মরণীয় ঘটনার সেই খাতাটিতে তিনদিন পর লিখেছেন। তার প্রথম ছত্রই হল—আজ তিনদিন ধরে ঘটনার আবর্তে পড়ে আমি কি পাল্টে যাচ্ছি? আজ তিনদিন আমি রাত্রে শোবার আগে মদ্যপান করিনি। একটা নতুন নেশায় যেন মেতে উঠেছি।
সেদিন হরিপ্রসাদজ্যাঠার বাড়ীতে জ্যাঠাইমার শ্রাদ্ধে গিয়ে কলকাতার বহু বিশিষ্টজনের সঙ্গে দেখা হল। পুরনো পরিচয় অনেকের সঙ্গে ছিল, তাদের সঙ্গে দেখাশুনো হয়নি আজ কয়েক বৎসর। পুরনো পরিচয় নতুন হয়ে উঠল। নতুন পরিচয়ও হল অনেকের সঙ্গে। কলকাতার দুই দলেরই বড় বড় মাতব্বররা এসেছিলেন। হরিপ্রসাদজ্যাঠা খুব হুঁশিয়ার লোক। ব্রাহ্মদলের কাছ-ঘেঁষা হয়েও দুই দলকেই সমান আদরে নিমন্ত্রণ করেছেন। ওদিকে পণ্ডিত-সভা বসেছে। পণ্ডিত-সভায় ভিড় খুব। রাজা রাধাকান্ত দেব ওখানে বসেছেন দেখলাম। তাঁর সঙ্গে তাঁর দলের হোমরা-চোমরারা। সংস্কৃত-জানা পণ্ডিত ব্রাহ্ম-ঘেঁষা কয়েকজনকেও দেখলাম। শুলাম, ওখানে তর্ক চলছে, বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয় বিচারের। বিদ্যাসাগর আসেননি। এলে আসরটা নিশ্চয় খুব জমত। ওদিকে যেতে সাহস হল না। পণ্ডিতদের টিকি নাড়া, নস্য নেওয়া আর সংস্কৃত বচন-ও আমার সহ্য হয় না। আমি বিধবা-বিবাহের দিকে।
ফটকেই দেবপ্রসাদদার শ্যালকের একটি ছেলে নিমন্ত্রিতদের গলায় বেলকুঁড়ির মালা পরিয়ে দিচ্ছিল। মালা পরে ভিতরে এসে দেখলাম, দেবপ্রসাদদার মেজ ছেলে শিবপ্রসাদ দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করছে। সে আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি এল প্রণাম করতে। বললাম—নিয়ে চল একবার শ্রাদ্ধের আসরে।
হরিপ্রসাদজ্যাঠা বসেছিলেন, প্রণাম করলাম। তিনি আমাকে আদর করে বসালেন কাছে। বললেন-এসেছ! আমি ভেবেছিলাম তুমি আসবে না।
ওই কথার মধ্যে অনেক কথা লুকানো আছে। আমি জানি। চুপ করে রইলাম। দেবপ্রসাদদা শ্রাদ্ধে বসে দান উৎসর্গ করছেন। দানগুলি ভাল হয়েছে। চারটে ষোড়শ
করেছেন। তাছাড়া একটা রূপোর ষোড়শ। জিনিসপত্রগুলো ভাল।
বললাম—দানগুলি চমৎকার হয়েছে।
হরিপ্রসাদজ্যাঠা বললেন—ইচ্ছা আছে স্ত্রী-শিক্ষার জন্য বিদ্যাসাগরমশায়ের হাতে এক হাজার টাকা দান করব।
—বিদ্যাসাগরমশায়কে দেখছিনে?
—তিনি কলকাতায় উপস্থিত নেই। থাকলে নিশ্চয় আসতেন।
এমন সময় কলকাতার সব থেকে উজ্জ্বল আলো (অবশ্য আমার কাছে) কালীপ্রসন্ন সিংহমশায় এসে দাঁড়ালেন। অনেকদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি, দেখা হয়ে খুব খুশী হলাম। তিনিও খুশী হলেন বলে মনে হল। আমাকে নমস্কার করে বললেন—রায়মশায়কে অনেকদিন পরে দেখলাম। ভাল আছেন জানি। খুব গানবাজনা নিয়ে মশগুল। তা বেশ। তা বেশ। তা বেশ।
হরিপ্রসাদজ্যাঠা শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। কালীপ্রসন্নবাবু এর পর সোফিয়াকে নিয়ে তাঁর সামনে রসিকতা করে বসবেন ভাবলেন—ওদিকে যে প্রসন্নকুমার ঠাকুরমশায় সিংহমশায়কে খুঁজছিলেন।
কালীপ্রসন্নবাবু বললেন—কেন মশায়, আমার সঙ্গে আবার প্রয়োজনটা কি হল তাঁর? আর তাঁকে তো দেখলাম না পণ্ডিত-সভার বিচারের আসরে!
হেসে হরিপ্রসাদকাকা বললেন—তাঁরা অন্যত্র বসেছেন। বৈঠকখানার একটা ঘরে। ওখানে খুব জোর আলোচনা হচ্ছে। বর্ধমানের মহারাজা লাখরাজের ব্যাপার নিয়ে যে মামলা করেছিলেন বিলেতে কোম্পানীর বিরুদ্ধে, তার রায় বেরিয়েছে। মহারাজা ডিগ্রী পেয়েছেন। সেই নিয়ে খুব আলোচনা চলছে।
হেসে কালীপ্রসন্ন বললেন—তাহলে বলুন, ল্যান্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের মিটিং বসে গেছে।
—তা বলতে পারেন। তবে যান একবার। বীরেশ্বরকেও নিয়ে যান। ওঁকেও খুঁজছিলেন। বলছিলেন, আপনার ভাইপো বীরেশ্বর রায় জমিদারী ভাল বোঝেন। তিনি আসেননি?
কালীপ্রসন্ন বললেন—চলুন রায়, দেখি। লাখরাজে স্বার্থ আমাদের সবারই, কম আর বেশী। আপনাদের আদি কর্তা তো শুনেছি প্রথম লাখরাজেই বিষয় পত্তন করেছিলেন। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ একশো বিঘে লাখরাজ নিলেমে ডাকিয়ে বলেছিলেন, এইবার শুরু কর।
আমি বললাম—হ্যাঁ।
***
ঘরটায় মোটা কার্পেটের উপর মজলিশ চলছিল। অধিকাংশই জমিদার এবং বেশ প্রতিষ্ঠাবান লোক। তার মাঝখানে প্রসন্নকুমার বসেছেন। তিনি ল্যান্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের বলতে গেলে জীবনীশক্তি। দ্বারকানাথের পর তাঁর এবং রাজাবাহাদুর রাধাকান্ত দেবের শক্তিতেই ওটা চলে। এই লাখরাজ বাজেয়াপ্তি নিয়ে আন্দোলন শুরু তাঁরাই করেছিলেন। আন্দেলনে কিছু হয়নি। বর্ধমানের রাজা মামলা করেছিলেন। এখানে হেরে বিলাত পর্যন্ত আপীল করেছিলেন।
একজন সংবাদ-প্রভাকরের মন্তব্য পড়ে শোনাচ্ছিলেন, প্রথমটা পড়া হয়ে গিয়েছিল, শেষভাগটা পড়া হচ্ছিল তখন।
“ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা এবং অন্যান্য নিষ্করভোগী মহাশয়েরা এইক্ষণে বর্ধমানেশ্বর বাহাদুরের জয়-জয় শব্দে আনন্দচিত্তে মুক্তকণ্ঠে আশীর্বাদ করুন। ওই ডিগ্রী সর্ব-সাধারণের পক্ষেই সমান কল্যাণকর হইয়াছে। যেহেতু তাহার তাৎপর্য এই যে, যে সকল ভূমির ৬০ বৎসর সমান ভোগ ও বিক্রয়-স্বত্বাধিকার প্রমাণ হইবে, তাহার দলিল দস্তাবেজ থাকুক না থাকুক, গভর্নমেন্ট কোনমতেই তাহার উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না।”
খিদিরপুরের ঘোষাল বললেন—ওটা তো গায়ের জোর ওদের। এ-দেশ নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর পীরোত্তর লাখরাজের দেশ। এ থেকেই দেবসেবা চলেছে। ব্রাহ্মণদের টোল চলেছে। মক্তব চলেছে। ওরা এসে দেশ দখল করে সবের উপরেই খাজনা চাপাবে। তা আইনে টিকবে কেন? ঠিক হয়েছে!
প্রসন্নকুমার আমাকে দেখে বললেন—আরে রায় যে। কিছুক্ষণ আগে তোমার খোঁজ কর ছিলাম তোমার কাকার কাছে! তুমি যে অদৃশ্য হয়ে গেলে হে। ল্যান্ডহোল্ডারস অ্যাসোসিয়েশনে প্রথম প্রথম যে কটি বক্তৃতা দিয়েছিলে তা বড় ভাল হয়েছিল। অনেক আশা করেছিলাম তোমার কাছে!
কালীপ্রসন্ন বললেন—উনি এখন সভ্য অ্যারিস্টোক্রাট মশায়। গ্রাম্য যখন ছিলেন তখন জমিদারী নিজের হাতে চালাতেন। প্রজাদের পিঠে ঠ্যাঙা চালাতেন, বুকে কাঠ চাপাতেন, বেঁধে রাখতেন, খাজনা আদায় করতেন, আবার নদীর বাঁধ বাঁধতেন, পুকুর কাটাতেন, গোচর ভাঙলে প্রজার জরিমানা করতেন, এখন শহরে বসে সভ্য হয়েছেন। জুড়ি হাঁকাচ্ছেন। একজোড়া কালো ঘোড়ার জুড়ি যা কিনেছেন চ-ম—কা-র! তারপর সন্ধ্যায় বাইজীর কণ্ঠে ঠুংরী টপ্পা শুনছেন। এখন আর খোঁজই বা কি রাখেন, বলবেনই বা কি?
আমি ছাড়লাম না, বললাম —কালীপ্রসন্নবাবু, এ ছাড়া আছে।
—কি বলুন। শুনি!
—মহাশয়ের লেখায় পড়েছিলাম—বাল্যাবধি ইচ্ছে কবি কালিদাস হব। কিন্তু সে ইচ্ছে ছেড়েছি কারণ কালিদাসের লাম্পট্য অনুসরণ করেও শক্তি না থাকলে কালিদাস হওয়া যায় না। তারপর ভেবেছিলাম, ঠিক মনে নাই সিংহমহাশয়, আপনি কি হতে চেয়েছিলেন, তবে তিনি নাকি দরিদ্রের পুত্র ছিলেন বলে সেটা হতে চান নি আপনি। আমি ভেবেচিন্তে লক্ষ্ণৌর ওয়াজিদ আলী শা হতে চেয়েছিলাম, দেখেছিলাম ওটা হওয়া যায়-ছোট আর বড়। ধরুন যেমন আপনি রামমোহন রায় হতে পারেন ধারণা ক’রে বিদ্যোৎসাহী হয়েছেন, গ্রন্থকার হতে চেষ্টা করছেন, বিধবা-বিবাহে উৎসাহ দিচ্ছেন। তেমনি আমিও ছোটখাটো ওয়াজিদ আলী শা হতে চাচ্ছি। তা সে তো গ্রামে বসে হওয়া যায় না। লক্ষ্ণৌ শহর অনেকদুর—কলকাতায় অন্তত না চেপে বসলে চলে কি করে?
কালীপ্রসন্ন উদার রসিক বলেই তাঁকে এত ভাল লাগে, এই কারণেই তিনি আমার কাছে কলকাতার নবীন সমাজের মধ্যে উজ্জ্বলতম মানুষ মনে হয়। তিনি আমার উত্তরে উচ্চহাস্য করে বললেন-ব্র্যাভো ব্র্যাভো, ব্র্যাভো রায়মশায়। চ-ম-ৎ-কা-র উত্তর দিয়েছেন। কথাটা প্রথম আলাপের দিনই আপনাকে বলেছিলাম আমি—নয়?
বললাম—দেখুন ঠিক মনে করে রেখেছি। তবে আমার মতো ক’রে ভেঙেচুরে নিয়েছি।
সকলেই মৃদু মৃদু হাস্য করতে লাগলেন।
প্রসন্নকুমার বললেন—না না রায়, আপনি অ্যাসোসিয়েশনে আসুন। সত্যিই জমিদারদের একটা বেশ সঙ্কট চলছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী যখন নিজে খাজনা আদায় করত তখন রেজা খাঁর দুর্নাম হয়েছিল। কিন্তু তার উৎসাহদাতা তো কোম্পানীর কর্তারা। হেস্টিংস সাহেব তো ঢালাও হুকুম দিয়েছিল। তারপর গুঁতো খেয়ে দায় চাপালে রেজা খাঁর উপর। রেজা খাঁ গেল—সঙ্গে সঙ্গে দেবী সিং, গঙ্গাগোবিন্দ সিং এলেন—তার সঙ্গে আপনার পিতামহও ছিলেন। তাঁরা যা করেছেন তাতে হেস্টিংসের হুকুম ছিল। আইনের পর আইন—পঞ্চম হপ্তম। প্রজাকে বেঁধে রেখে মারধর করে খাজনা আদায় করে দাও, আমাদের পেট ভরাও, কোম্পানীর ক্যাশে চালান যাক। তারপর পারমানেন্ট সেটেলমেন্ট। দশ ভাগের ন ভাগ—শতকরা নব্বুই টাকা কোম্পানীর প্রাপ্য। বাস যেই পারমানেন্ট সেটেলমেন্ট হয়ে গেল, একটু সুরাহা হল, অমনি বাতিল হল পঞ্চম হপ্তম। কোম্পানীর সমদৃষ্টি। প্রজাকে মারধর করতে দেবেন না। তারপর পারমানেন্ট সেটেলমেন্টের সুবিধের জন্যে অষ্টম আইন। ভাল কথা। বেশ কথা। তারপর লিমিটেশন অ্যাক্ট। এদেশে সুদ ছিল না তামাদি ছিল না। এখন তামাদি—চার বছরে কর নালিশ। পাঁচ বছরের খাজনা পাবে। কোম্পানীর লাভ হবে স্ট্যাম্প। আবার সব নতুন আইন হচ্ছে। প্রতীক্ষায় থাকুন। ওদিকে ভারতগ্রাস চলছে। একে একে সব পেটে ভরছে। লর্ড অকল্যান্ড, লর্ড এলেনবারা, তারপর লর্ড ডালহৌসি। মারাঠা ঝাঁসি খেয়ে ফেলেছে। এবার, এই এক্ষুনি বলছিলেন লক্ষ্ণৌর ওয়াজিদ আলী শার কথা। তার কি হচ্ছে দেখুন। তাকে হটিয়ে বোধ হয় অযোধ্যা নিলে বলে!
মজলিশটা অকস্মাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেল। সকলে চুপ ক’রে বসে রইলেন। হঠাৎ ওঘরের কথাগুলো কানে এল। ভূত! ভুত! ভুত!
কালীপ্রসন্ন বললেন—ঠাকুরমশায়, ওঘরে দেখছি ভূত নেমেছে। আমি আর রায় একটু ভৌতিক কৌতুক উপভোগ করে আসি। বলে আমাকে টানলেন।
.
ওঘরে মজলিশ সত্যই জমজমাট। তামাকের আসরে তামাকবিলাসীরা বসেছেন, গড়গড়া ফুরসী হরদম তাজা, রূপো বাঁধানো হুঁকোর মাথায় বিশটা কল্কেতে কাষ্টগড়া, বিষ্টুপুরী-গয়ার তামাক পুড়ছে। আতরের খুসবাই ভুরভুর করছে। রূপোর পরাতে বিস্তর পানের খিলি। পান মুখে তামাক টানতে টানতে মল্লিকদের রাম মল্লিক গল্প বলছেন
কালীপ্রসন্ন বললেন-বেড়ে জমিয়েছ মল্লিক।
মল্লিক তুখোড় লোক, বললে—মিছরির দানার ছুরির মুখটা জমতে বাকি ছিল, সিং, তুমি এয়েচ বাবা, এবার দানা পুরো জমাট হয়ে গেল। এস।
—এলাম। কিন্তু আচ্ছা ভূত নামিয়েছ তো। ওঘর থেকে ঘাড়ে ধরে নিয়ে এল হে। বল গল্পটা শোনা যাক।
—গল্প নয় বাবা। সত্য। তাঁবা-তুলসী গঙ্গাজল-জর্ডনের জল-গীতা-বাইবেল হাতে বলতে পারি। আমার জ্ঞাতিভাই সুরেন্দ্র মল্লিক, যাকে লোকে বলে স্যাণ্ডার মালিক, যে পাদরীদের কাছে যাওয়া-আসা করে। ক্রীশ্চান হই-হই করছে, লোভ মেমের উপর নিদেন দেশী পাদরী- কন্যা। তার বাবা মারা গেছে মাস তিনেক। শ্রাদ্ধ করেনি। এখন বাপ ভূত হয়েছেন। ঠ্যালা নাও। ইংরিজী বিদ্যে বাক্যি বেরিয়ে গেছে। বাছাধন কাঁপছেন। বুঝলে না, রাত্রিকালে এক- দিন নয়, দুদিন নয় চারদিন এই রাত ঠিক বারোটা একটা বাজে আর ঘরের বাইরে কেউ যেন ঘুরে বেড়ায়—দরজা হুট্হাট্ করে মনে হয়। বাস্ ঘুম ভেঙে যায়। প্রথম মনে করেছিল চোর। নয়, ঘরে তো দাসী-টাসী আছে আর ছোঁড়া চাকরও আছে। ঠাকুর আছে, আমলা আছে। তা ঘর খুলে বেরিয়েও ছিল। সাহস আছে আমাদের সুরেন্দরের। তা বলতে হবে। একটা গুপ্তি হাতে বেরিয়েছিল। কোথায় কি? কাক পড়ে বেদানা খাচ্ছে মানে কাকস্য পরিবেদনা। তারপর ভাবলে ইঁদুর-টিদুর। ঘরের দরজা বদ্ধ করেছে আর বাইরে থেকে—
নিজেই নাকিসুর করে মল্লিক বললে—সুরন্দর! সুঁরো!
এবার সহজ সুরে মল্লিকই সুরেন্দ্র হয়ে বললে-কে?
—আঁমি তোঁর বাঁবা। বড় কঁষ্ট। ছেঁরাদ্ধ করিস নি। পেরেত হয়ে বড় কষ্ট পাচ্ছি। আঁমি মরবার ক্ষণে তিনঁ পোঁ দৌঁষ পেঁয়েছি। ছেঁরাদ্দ কর। দোঁষ কাঁটা। নইলে পেঁরেত হয়েছি। রাঁগ হচ্ছে। ইচ্ছে হচ্ছে তোঁর বুকে চেঁপে বসি—গলাটা টিপে দি।
প্রায় সমস্বরে শব্দ উঠল—ওরে বাবা! তারপর?
মল্লিক বললে—তারপর আর কি। চক্ষু চড়ক গা-ছ! হস্তপদ গুটিয়ে পেটের ভিতর। বু-বু-বু-বু শব্দ করে ধপাস করে পতন! শব্দ শুনে বউ জেগে ওঠে—সেও ক’রে বু-বু। শেষে বাড়ীর লোক—তার পরেতে পাড়ার লোকের জাগরণ। কি ব্যাপার? কি ব্যাপার মশায়? না—ও কিছু না। কি রকম একটা বাইরে শব্দ হতে ভয় পেয়ে গেলাম। বুঝুন, ছোকরার ধড়িবাজিটা একবার বুঝুন। এর পরেও বলে-ও কিছু না। কিন্তু যাবেন-টা কোথায়? বাছাধন যাবেন-টা কোথায়? পরের দিন ঠিক আবার খুটখাট হুট-হাট! আর নাকিসুরে-সুরন্দর শেষ গঁলাই টেপাবি? বাস্ এই একটি কথা! এমনি তিন-চারদিন। এখন বাছাধন যাচ্ছেন দেশ বেড়াতে। মানে গজং গচ্ছ গয়াং গচ্ছ। গয়া যাচ্ছেন। সেখানে শেরাদ্ধ পিণ্ডি সব শেষ করবেন। মাথা কামাতে হবে তো। তা মাথায় চুল না গজানো পর্যন্ত এদিকে ওদিকে ঘুরে দেশে ফিরবেন। বুঝলে না? শেরাদ্ধও হবে পাদরীদের কাছেও মুখ থাকবে! তা আমিও বাবা রাম মল্লিক, তাকে তাকে আছি, ও যেদিন রওনা হবে, আমিও রওনা হব পিছু পিছু। চল না, কোথায় যাবি চল না। ঠিক পিছন পিছন যাব আমি।
কালীপ্রসন্ন বললেন-মল্লিকমশায়ের শেষ খবরটা ভুল। মানে ও গয়াটয়া কোথাও যাচ্ছে না।
—এখানেই শ্রাদ্ধ করবে নাকি তা হ’লে?
—না। পাদরী সাহেবদের কানে কথাটা উঠেছে। তারা ওকে বলেছে, don’t be afraid মালিক, don’t worry, আমি আজই মাদার মেরীকে বলিটেছি, মাদার আপনি আদেশ করেন, দো গোরা পল্টন ভূট পাঠাইয়া ডিন। ব্ল্যাকহোল ট্র্যাজেডি হইটে যারা মারা গেল, টারা ভুট হইয়া আছে। টারা সঙ্গীন লইয়া রাত্রে পাহারা ডিবে, উ বাবা ভুটটা আসিলেই গ্রেপ্টার করিয়া হোলি গোস্টের কাছে লইয়া যাইবে। হোলি গোস্ট বাবা ভূটটাকে কিরিশটান করিয়া ডিবে।
মল্লিক তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল।—তামাশা। কিন্তু তামাশা বেরিয়ে যাবে সিংহমশায়।
—তামাশা নয়। আমি যা শুনেছি তাই বলে গেলাম। কালীপ্রসন্ন অত্যন্ত গম্ভীরভাবে কথা ক’টি বলে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।
মল্লিক বললে—পা-ষ-ণ্ড!
ঠিক এইসময় বাড়ির চাকর এসে রায়কে বললে—রাণীমা একবার ডাকছেন আপনাকে অন্দরে।
রাণীমা অর্থাৎ দেবপ্রসাদদার স্ত্রী। জগদ্ধাত্রী বউদি। ভবানীর সখী। বয়সে ভবানীর থেকে দু’তিন বছরের ছোট। অনেকদিন দেখা হয়নি তাঁর সঙ্গে। ভবানীর নিরুদ্দেশ বা মৃত্যুর পর থেকে আর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। দেবপ্রসাদ যায়নি তাঁর বাড়ি। তিনিও এ-বাড়ী আসেননি।
***
জগদ্ধাত্রী বউঠাকরুণ নিজের ঘরে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি ঘরে ঢুকবামা বললেন—এস ঠাকুরপো! বস।
—ভাল আছ বউদি? ব’লে হেঁট হয়ে প্রণাম করতে গেলেন রায়।
জগদ্ধাত্রী পিছিয়ে গিয়ে বললেন—ওকি? আজ কি নতুন হলাম নাকি! কবে তোমার প্রণাম নিয়েছি!
—নাওনি, তখন আর একটা ব্যাপার ছিল। সে তো চুকে গেছে। এখন নেবে না কেন?
–না। তা হ’লেও না। মানুষ ম’রে গেলেও সম্পর্ক একবার হ’লে চোকে না ঠাকুরপো। আমি যদি মরে যাই তবে ওঁর কি আমার বাপ-মা ভাইদের সঙ্গে সম্পর্কটা মুছে যাবে? বস।
চেয়ার পাতা ছিল। সামনে মার্কেলটপ টেবিলে রূপোর রেকাবিতে কিছু খাবার এবং রূপোর গ্লাসে জল রাখা ছিল। জগদ্ধাত্রী বউদি বললেন—খাও। একটু জল খাও। এ বাড়ীতে তো তুমি আসই না। আজ সাত আট বছর কলকাতায় এসেছ, কখনও আস না, কোনও একটা খবরও দাও না। আমি যেতে পারিনে
লজ্জায় কথাটা বলতে পারলেন না জগদ্ধাত্রী বউদি।
রায় বললেন—যাওনি ভালই করেছ বউদি। যে বীরেশ্বর রায়কে গিয়ে দেখতে সে এক কি বলব? প্রেত বলতে পার-নরক-বিলাসী বলতে পার!
চুপ করে রইলেন জগদ্ধাত্রী। একটু পর বললেন—তুমি খাও ভাই। আমি জানি তুমি এই এসে চলে যাবে, আর আসবে না। এসেছ এই মহাভাগ্যি বলতে হবে। খবর পেয়ে সেইজন্যেই আমি শত কাজ ফেলে আজ তো ভাই হাজার কাজ বুঝতেই পারছ, —সব ফেলে তোমাকে ডাকতে পাঠিয়েছিলাম। একবার দেখা করব। একটু মিষ্টিমুখ করাব। আর দুটো কথা বলব। নাও হাতে আমিই জল দিচ্ছি। ইচ্ছে করেই দাসীচাকর কাউকে রাখিনি। যে কথা বলব—তা কারুর সামনে হয় না। নাও, তোয়ালে ধর, মুখ মোছ। খাও। আমি বলে নিই কথাটা। না বলে প্রাণটা আনচান করছে আমার।
মুখে দু টুকরো ফল ফেলে দিয়ে তাঁর মুখের দিকে সবিস্ময়ে তাকালেন বীরেশ্বর।—এমন কি কথা বউদি? তার কথা?
—একরকম তাই। সে নেই—
—সে মরেছে?
—মরেছে বইকি? নইলে কি খবর পেতে না?
—খবর টুকরো টুকরো পাই বউদি। কাল রাজা রাধাকান্ত দেবের বাড়ী গিছলাম। শুনলাম তাঁর ওখানে বিমলাকান্ত কিছুদিন কাজ করেছিলেন। তার ওখানে একজন কেউ ছিল তাঁর ভগ্নী! বিমলাকান্তের ভগ্নী তো কেউ ছিল না বউদি। সে তো সবাই জানে। সে ছাড়া আর কে হবে বল? সে তাকে দাদা বলত—
—না ঠাকুরপো, তুমি তাকে ভুলেই যাও। সে মরেছেই ধর। তুমি বিয়ে কর।
—সে মরলে বিয়ে করতে পারি বউদি। বেঁচে থাকলে তাকে আমি খুন করব, তারপর ফাঁসি যাব। একটা নিরপরাধ মেয়েকে বিধবা ক’রে কি লাভ হবে বল?
—তোমার মনের কথা যা তা আমি জানি।
–কি জান?
—তোমার সন্দেহের কথা আমি জানি।
চমকে উঠলেন বীরেশ্বর। এ কথা জানেন তিনি আর সে—পৃথিবীর আর কাউকে জানতে তিনি দেননি। তবু স্বাভাবিক ভাবে জেনেছিল বিমলাকান্ত। তার জানারই কথা। সেই তাকে বলেছে? কিন্তু জগদ্ধাত্রী বউদিকে কে বললে? কে বলতে পারে! তেমন চমকে উঠে ঘাড় তুলে জিজ্ঞাসা করলেন—কে বললে তোমাকে?
দরজার মুখে একজন ঝি এসে দাঁড়াল, জগদ্ধাত্রীকে ডাকলে-বউরাণীমা!
—কি?
—নিচে বড় গোলমাল। আপনি আসুন। পিসীঠাকরুণ চেঁচামেচি করছে—যত সব মেলেচ্ছোর কাণ্ড-তিনি চলে যাবেন। এখুনি চলে যাবেন!
জগদ্ধাত্রী বললেন—আমি যাচ্ছি তুই যা।
বলে ওপাশে গিয়ে দেওয়ালের ধারে রাখা একটা বড় চেস্টড্রয়ার খুলে তার ভিতর থেকে একখানা চিঠি এনে বললেন—চিঠিখানা পড়ে দেখো। মাসখানেক আগে চিঠিখানা পেয়েছি!
চিঠিখানার খামের উপরের হস্তাক্ষর দেখে তাঁর মাথা ঝিমঝিম্ করে উঠল। এ লেখা—ভবানীর হাতের লেখা!
***
সুরেশ্বর বললে—ঠিক এই সময়ে মেজঠাকুমা ঘরে ঢুকলেন সুলতা। বললেন—এখনও আলো জ্বেলে কি পড়ছিস সুরো? রঘু বললে—কাল ও-বাড়ী থেকে গানটান ক’রে এসে সেই আলো জ্বেলে পড়তে বসেছিস, সকাল হয়ে গেছে তবুও পড়ে যাচ্ছিস। খাস নি দাস নি। রঘু ভয়ে তোকে ডাকতে পারে নি।
সুরেশ্বরের মোহ ভেঙেছিল। সে এতক্ষণে ঠাওর করেছিল যে সে বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে ১৯৩৬ সালে কীর্তিহাটের পুরনো বাড়ী বিবিমহলে বসে দুর্দান্ত বীরেশ্বর রায়ের স্মরণীয় ঘটনা লেখা খাতাখানা পড়ছিল। অতীতকালের মধ্যে সে চলে যায়নি!
খাতাখানা বন্ধ করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। ভবানী দেবী তাঁর পত্রে জগদ্ধাত্রী দেবীকে কি লিখেছেন তা জানবার জন্যে চিত্ত আমার অধীর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু মেজঠাকুমার পিছন পিছন—ভাই রাজা! বলে ডাক দিলে ব্রজেশ্বরদা!
যত মিষ্ট ব্রজেশ্বরদাদা-তত পচা; না- সুলতা ঠিক হল না। ব্রজেশ্বরদা উৎকৃষ্ট মদ্যের মতো। যখন খাই তখন মনেই সুধা, তারপর তার যখন ক্রিয়া হয় তখন মনে হয় সে বিষ এবার তাকে মনে হচ্ছিল পুরনো অনেক পুরনো মদের মতো। তার স্বাদ বেড়েছে। নেশাতে বিষের ঝাঁঝ কমেছে। ভবিষ্যতে পোর্ট-টোর্টের মতো সব বিষটুকু উপিয়ে দিয়ে ওষুধ হয়ে উঠতে পারে—তাহলে বিস্মিত হব না!