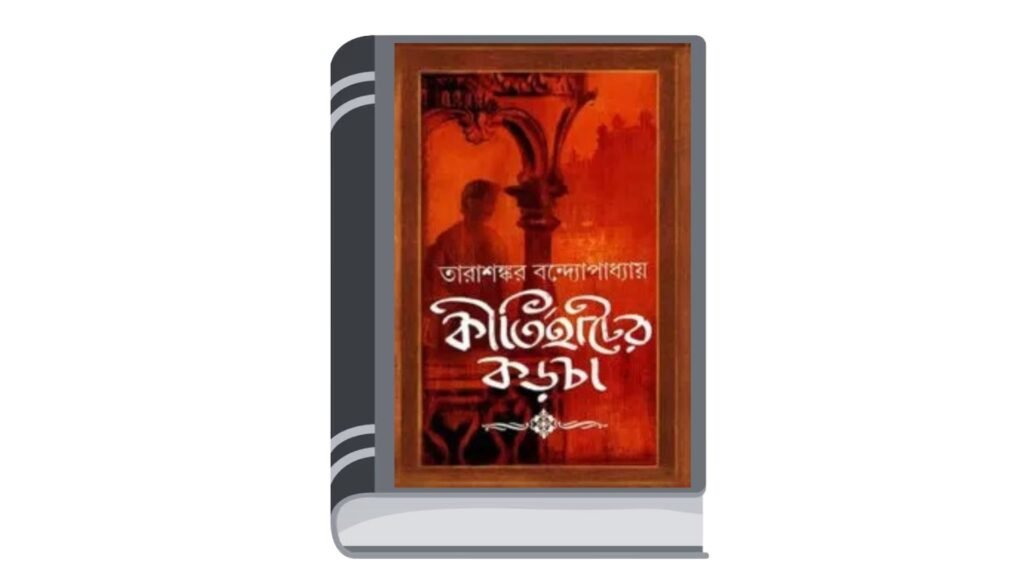কীর্তিহাটের কড়চা – ৩য় খণ্ড – ১২
১২
সুরেশ্বর বললে—গোপাল সিংয়ের পৌত্র হরি সিংয়ের উপর শোধ নিতে পথ খুঁজতে আমাকে চিন্তা করতে হয় নি। বিমলকাকা এমন শান্ত লোক হয়েও ভুল করে বীরেশ্বর রায়ের পথ নিয়েছিলেন। আমি রত্নেশ্বর রায়ের নির্দিষ্ট পথ নিয়েছিলাম নির্ভয়ে। ইংরেজ সরকার তাকে রক্ষা করতে চাচ্ছে কিন্তু পারবে না। আমি তার উপর কিস্তি কিস্তি নালিশ করব। ইংরেজকেই আমাকে ডিক্রীদিতে হবে। তার আদালতের পেয়াদারা এসে তার যথাসর্বস্ব ক্রোক করবে। সে যাবে কোথায়?
সুলতা, আমার মনে আছে, সেদিন মনে জমিদারীর নেশা লেগেছিল, আমি রঘুকে বলেছিলাম- দে রঘু, বোতলটা দে।
সুলতা বললে—তোমার জমিদার গৌরব পরে শুনব, কিন্তু রত্নেশ্বর রায় দুটো লোককে খুন করিয়েছিলেন বলছিলে। সে জমিদারীর জন্য নয় বলছ তুমি?
সুরেশ্বর বললেনা সুলতা, জমিদারির জন্য নয়, যে দুটো খুনই তিনি করিয়েছিলেন তার কোনটাই জমিদারীর প্রয়োজনে করেন নি। সংসারে রাম-রাজত্বের কথাও আছে, রাবণ-রাজত্বের কথাও আছে।
বাঁকা হেসে সুলতা বললে-কি বলছ তুমি? রত্নেশ্বর রায় দুটো খুন করিয়েছিলেন, রামচন্দ্রের সীতা-নির্বাসন এবং শুদ্রক-তপস্বী-বধের মত পুণ্যকর্ম ভেবে করেছিলেন?
—কথাটা তুমি অনেকটা ঠিকই বলেছ সুলতা। রামচন্দ্র রাজা না হলে এ দুটো করতেন না। আমার কথাটা আমি শেষ করি নি; তুমি তার আগেই মন্তব্য করেছ। রামচন্দ্র রাজা না হলে—সীতাকে সতী জেনেও পরের মিথ্যা সন্দেহে নির্বাসন নাও দিতে পারতেন। আর শুদ্রক তপস্যা করার দরুণ অনাবৃষ্টি হয়েছে, এর জন্য তাকে শাস্তি তিনি দিতেও পারতেন আবার নাও দিতে পারতেন। অনেক মানুষ আছে যারা রাজা নয় জমিদার নয়, তাদের মধ্যে অনেকে স্ত্রীকে হরণের জন্যে—যে হরণ করে তাকে খুন করে, অনেকে আর এক বিয়ে করে দিব্যি সুখেস্বচ্ছন্দে থাকে, আর পাড়ার বা গ্রামের বদমাশকে কেউ কেউ শাস্তি দেওয়ার ভারটা কর্তব্যবোধে ঘাড়ে তুলে নিয়ে দাঙ্গা-মারপিট করে হাঙ্গামা বাধায়, জেলেও যায়। কিন্তু রাজা হলে ওই রামের মতই কাজ না করে উপায় থাকে না।
—তার মানে?—
—ধর, ঠাকুরদাস পাল রায়বংশের গোপন পাপের কথা প্রকাশ করব বলে ভয় দেখিয়েছিল। এক্ষেত্রে রত্নেশ্বর রায় সাধারণ লোক হলে তার সঙ্গে হাতাহাতি করতে পারত আবার মুখ বুজে সয়েও যেতে পারত। কিন্তু জমিদার রত্নেশ্বরের ঠাকুরদাস পালের মুখ বন্ধ না করে উপায় ছিল না। ওটা জমিদারী রক্ষার জন্য বা জমিদারীর আয় বাড়াবার জন্য নয়। ওটা জমিদার হওয়ার জন্য। দ্বিতীয় খুনটাও তাই। একজন গোয়ানকে তিনি কোথায় হারিয়ে দিয়েছিলেন, সে কেউ জানে না।
—রায়বাড়ীর মর্যাদা?
—রত্নেশ্বর লিখেছেন তাই তাঁর ডায়রীতে। কিন্তু ঠিক তা নয়। অঞ্জনা যদি ভ্রষ্টাই হয়ে থেকেছিল, তাতে রায়বাড়ীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবার কথা নয়। অথচ এটাকে তিনি তাইই ভেবেছিলেন! ওই ছবিখানা আর একবার দেখ সুলতা। ওই যে বিবাহের ছবির পর, যেখানে রত্নেশ্বর রায়, স্বর্ণলতা দেবী বিদ্যাবতী বউ, এবং অঞ্জনা তিনজন রয়েছে, সেখানার দিকে। অঞ্জনা বলছে-বিদ্যেবতী না—নাম থাকুক সরস্বতী বউ। জ্যাঠাইমা সতী বউ, তার বেটার বউ সরস্বতী বউ। বিদ্যেবতী যেন ঠাট্টা-ঠাট্টা। বিদ্যেসুন্দরের বিদ্যে-বিদ্যে।
—মেয়েটি তো লেখাপড়া জানত না বলছ।
—কিন্তু বলেছি ছড়া, পাঁচালী, এসব মুখস্থ ছিল, বিদ্যাসুন্দর সে আমলে খুব চল ছিল। কে তাকে পড়িয়ে শুনিয়েছিল জানি না। তবে বিদ্যাসুন্দর কারুর কাছে সে শুনেছিল। এখানেই স্বর্ণলতা বলেছিলেন—কর্তা গিন্নীকে বলে অঞ্জনাকে আমাকে দাও। ওঁরা তো শুনেছি এইবার কলকাতা যাচ্ছেন। তারপর যাবেন পশ্চিম। কাশী গয়া বৃন্দাবন তীর্থ করতে। ওরই মধ্যে রত্নেশ্বর রায়ের ওই গোয়ানটার হারিয়ে যাওয়ার বীজ লুকিয়ে আছে।
সুরেশ্বর বললে—এই দুটো খুনের যা কারণ তা জমিদারীর প্রজাশাসন, প্রজাশোষণ এ সবকিছুর জন্য নয়, এর কারণ যা তা জীবনে অনেকের ঘটে থাকে, হয়ে থাকে। মা-বাপের নামে কেলেঙ্কারি অপবাদ রটনা করলে এ কাজ ক্রোধবশে যে-কোন লোক করতে পারে। তবে জমিদার বলে রত্নেশ্বর রায়ের পক্ষে সহজ হয়েছিল, যদি বল স্বাভাবিক হয়েছিল, তবে তাতেও আপত্তি করব না।
আর এই গোয়ানের ব্যাপারটা ওটাও তাই বলা যায়—তবে ওর আসল কারণটা অন্য, দেখেছ, রত্নেশ্বর রায়ের দৃষ্টি অঞ্জনা এবং স্বর্ণলতার মাঝখানে একটা মাকড়সা ছাদ থেকে সুতো টেনে নামছে সেটার দিকে? দেখ সুতোটা দুলছে, ছাদ থেকে রাইট অ্যাংগেল করে নেমে আসেনি, একটুখানি বেঁকে আছে।
সুলতার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বললে—তুমি ওটা বড় ভাল কল্পনা করেছ সুরেশ্বর। মাকড়সাটা অঞ্জনার দিক ঘেঁষে বেঁকে রয়েছে। তুমি কি—।
সুরেশ্বর বললে—হ্যাঁ। তাই।
—রত্নেশ্বর সাধুতার আবরণে—
—না, আবরণে নয়। ওটার ইন্টারপ্রিটেশন অন্যে যে যা করবে করুক আমি তা করি নি। তা করব না। কখনো না। রত্নেশ্বর রায় নিজের জীবনে কোন অসাধুতা কোন অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন নি। মানুষ তিনি, তাঁর মনও মানুষের মন, তাঁর মনে যখনই কোন অন্যায় অসাধু প্রবৃত্তি উঁকি মেরেছে, তখনই তাকে তিনি চাবুক মেরে সার্কাসের ট্রেনার যেমন বাঘ সিংহকে খাঁচায় ঢোকায় তেমনি করেই তাদের পিঞ্জরেতে পুরেছেন। নির্মম ভাবে নিজেকে আঘাত করেছেন, তিরস্কার করেছেন।
এর ইন্টারপ্রিটেশন আমার কাছে এই রায়বাড়ীর রক্তে শ্যামাকান্ত এবং সোমেশ্বরের ধর্মসাধনায় ভ্রষ্টতার পাপ। শ্যামাকান্ত যেমন শেষজীবনটা ক্রমাগত নিজেকে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত ক’রে শাসন করতেন, ঠিক তেমনি ক’রেই রত্নেশ্বর রায়ও নিজের অন্তরের মধ্যে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করেছেন। এই পাপই বল আর তোমাদের আজকের ইন্টারপ্রিটেশন অনুযায়ী হেরিডিটিই বল, অথবা এইটেই মানুষের স্বভাবের আসল চেহারাই বল, বলতে পারো। কিন্তু আমি তা বলব না।
রত্নেশ্বরের জীবনে এই শাপ বা পাপকে প্রথম উদ্রিক্ত করেছে এই অঞ্জনা। একটু আগে বলছিলে—অঞ্জনার মুখের ঢঙের মধ্যে, আকৃতির মধ্যে আর কার ছবির যেন ছাপ পড়েছে।
পড়েছে সুলতা, একজনের নয় দুজনের। রায়বাড়ির কড়চা বা জবানবন্দীতে প্রথম এ মুখের ছাপ পাবে সেই পাগল মেয়েটির মধ্যে, যাকে শ্যামাকান্ত চিনেছিলেন যোগিনী বলে। যাকে নিয়ে তিনি কাঁসাইয়ের ওপারের সিদ্ধপীঠের জঙ্গলে সাধনার নামে ব্যভিচার করেছিলেন। এবং শ্যামাকান্তকে সেই বর্ষার সময় অমাবস্যার রাত্রে দারুণ দুর্যোগে তুফানপ্রমত্তা কাঁসাইয়ের জলে ফেলে দিয়ে সোমেশ্বর তাকে কেড়ে নিয়েছিলেন যোগিনী সাধনা করবেন বলে। চল, ওইদিকে চল, তার ছবি দেখবে। মিলিয়ে পাবে। তুমি আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলে, কিন্তু তখন কথাটা এড়িয়ে গিয়েছিলাম।
—এই দেখ, পর পর দুখানা ছবিতে যে পাগলী এসে রায়বাড়ীর দরজার সম্মুখে দাঁড়িয়েছে। ধুলিধূসর দেহ, অর্ধউলঙ্গ, মাথায় একরাশ ঝাঁকড়া চুল। এর সঙ্গে হয়তো পুরো মিল পাবে না। কিন্তু এইটেতে পাবে। এই দেখ, পাগলাবাবা শ্যামাকান্ত তাকে খাইয়ে-দাইয়ে সুস্থ করেছে। স্নান করিয়েছে। নতুন কাপড় পরিয়েছে। মেয়েটি শান্ত এবং তৃপ্ত হয়ে শ্যামাকান্তের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছে। আরো দুটো ছবি আছে, এই একটা দেখ সোমেশ্বর রায়ের অন্দরে, সোমেশ্বরের কন্যা বিমলাকে কোলে করে দোলাচ্ছে। কী প্রসন্ন শান্ত মুখ দেখ! আর একটা ছবি, যোগিনী তখন সোমেশ্বরের সাধনসঙ্গিনীর ছদ্মবেশে তাঁর বিলাসসঙ্গিনী হয়েছে, দেখ, এইটেতে যে ছবি আছে তারই সঙ্গে অঞ্জনার মিল রয়েছে পুরো।
সুলতা দেখলে। তাই বটে। দেখলে ভ্রম হয়; মনে হয় বুঝি যোগিনীই দাঁড়িয়ে আছে রত্নেশ্বরের সামনে। একটু ভেবে নিলে সুলতা। কপালে ক’টা রেখা জেগে উঠল। একটু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললে—এটা তুমি কেন করলে সুরেশ্বর? অঞ্জনা রায়বাহাদুরের পোষ্য ছিল—হয়তো বা
—না সুলতা, তা ছিলেন না অঞ্জনা দেবী।
—তা হলে দুটো ছবি একরকমের ক’রে তুমি ওই মেয়েটির কি অপমান কর নি?
—না। তুমি রাগ করো না। একটু ভেবে দেখ। এখানে ওই মেয়েটি রায়বংশের কড়চার একটা সিম্বল। আমি যোগিনীর কোন ছবি পাই নি। দেখি নি। অঞ্জনার একটা ফটো ছিল শুনেছি কিন্তু সেটা নাকি রায়বাহাদুর আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। তবে এক জায়গায় তার ছবির আদল পেয়েছি। তাই দেখে অঞ্জনার ছবি এঁকেছি। এবং তা থেকেই যোগিনীর ছবিও এঁকেছি। আগে আমার জবানবন্দী শেষ হোক, তারপর তুমি রায় দিয়ো। তবুও যদি তর্ক করো তবে কৈফিয়ত হিসেবে বলব- বিজ্ঞানস্বীকৃত একটা নিয়মকে আমরা সৃষ্টির মধ্যে লক্ষ্য করি, সেটা হল একজনের সঙ্গে আর একজনের আশ্চর্য চেহারার মিল। ওটা হয়ে যায়। এও তাই।
একটু বক্র হাসি সুলতার মুখে ফুটে উঠল।
সুরেশ্বর বললে—তুমি এখনও বিচারক হিসেবে নিরপেক্ষ হতে পারলে না। কিন্তু পরে তোমাকে মত বদলাতে হবে।
—ভাল। বল শুনি!
একটু চুপ ক’রে বোধহয় কিছু ভাবলে সুরেশ্বর, তারপর বললে—তা’হলে তোমাকে রায়বংশের জবানবন্দীর ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ করে পাঁচ বছর পরে যা ঘটেছিল সেইটেই আগে—এখনই শুনিয়ে দিই। আমি আমার কথায় বলব না। বলব রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীর কথা।
সামনের টেবিলের উপর রাখা ডায়রীগুলির গাদা থেকে ১৮৬৪ সালের ডায়রী বেছে নিয়ে দেশলাইয়ের কাঠি পোরা চিহ্নিত জায়গাগুলি খুলে দেখতে দেখতে একজায়গায় থামলে সুরেশ্বর। বললে-এই পেয়েছি। শোন।
“আমি নিভৃতে রুদ্ধদ্বার কক্ষে অঞ্জনাকে ডাকিয়া কঠিন ভান করিয়াই কহিলাম-এ তুমি কি করিতেছ? এসব কি শুনিতেছি?”
অঞ্জনা ভয় পাইল না, সে বলিল—কী শুনিতেছ?
—তুমি জান না? গোটা অন্দরে কথাটা লইয়া কানাকানি চলিতেছে। লোকে হাস্য করিতেছে।
—কানাকানি চলুক। হাস্য করুক—তাহাতে আমার কিছু আসে যায় না।
আমি এবার রোষদৃপ্ত কণ্ঠে কহিলাম —অঞ্জনা, তুমি সাবধান হইয়া কথা বলিবে।
অঞ্জনা আশ্চর্য এক হাস্য করিল, যেন জগৎসংসার সমস্ত কিছুকে অবজ্ঞা করিয়া কহিল- কেন? কি করিবে তুমি? মারিয়া ফেলিবে? তোমরা বড়লোক জমিদার, তোমরা সব পার। কিন্তু আমি তাহাতে ভয় করি না। আমি তাহাতে জুড়াইব। তবে একটি দয়া প্রার্থনা করিব। যেন ভাড়াটিয়া লোক দিয়া আমাকে হত্যা করাইয়ো না। তুমি স্বহস্তে আমাকে হত্যা করিয়ো। তুমি বিষ গুলিয়া আমাকে দিয়ো, আমি সহাস্যে তাহা পান করিয়া মরিব। তুমিই আমাকে লিখিতে পড়িতে শিখাইয়াছ, আমি স্বহস্তে লিখিয়া যাইব, আমি স্বেচ্ছায় বিষপান করিয়া মরিতেছি। ইহার জন্য কেহ দায়ী নহে।
অঞ্জনা প্রগল্ভা বটে। কিন্তু এরূপ দুঃসাহসিক প্রগল্ভতায় আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম —অঞ্জনা, তুমি পাপিনী। কালসপিনীর সহিতই একমাত্র তোমার তুলনা হয়। দুগ্ধ পান করাইয়াও ফল হইল না।
অঞ্জনা এবার যেন আরো উদ্ধত এবং প্রগল্ভ হইয়া বলিল—হাঁ হাঁ—আমি কালসপিনীই বটে। আমি পাপিনীই বটে। পাপ উদ্দেশ্যেই তোমাদের গৃহে সেবার আসিয়াছিলাম। দরিদ্রের কন্যা, এক দরিদ্রের স্ত্রী, সে দরিদ্র হইলেও ক্ষতি ছিল না, সে পাষণ্ড, সে দুশ্চরিত্র, সে বাউন্ডুলে। তোমাদের গৃহে আসিলাম উৎসব দেখিতে। ঐশ্বর্য দেখিয়া লোভ হয় নাই তাহা বলিব না। অত্যন্ত লোভ হইয়াছিল। কিন্তু ততোধিক লোভ হইল তোমাকে দেখিয়া। আবার ভয়ও হইল। তোমার মত গম্ভীর, তোমার মত কঠোরচরিত্র যুবক আমি দেখি নাই। পিত্রালয়ে, আমার দিকে আমাদের গ্রামের দুশ্চরিত্র যুবকেরা লোলুপদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিত। আমি কৌতুক বোধ করিতাম এবং অহংকারও অনুভব করিতাম। তাহাদিগকে লইয়া কথার খেলা করিতাম। আমি কালো হইলেও আমার মত মোহময়ী যুবতী দুর্লভ ইহা আমার অজ্ঞাত ছিল না। রাজার ঘরে আমি পড়িলে তোমার স্বর্ণলতা অপেক্ষা বহুগুণে মহীয়সী হইতে পারিতাম। তুমি প্রথম আমার দিকে একবার চাহিয়া আর ফিরিয়া চাহ নাই। তারপর তোমার মাতা অনুগ্রহ করিয়া গৃহে স্থান দিলেন। আমি হস্তে চাঁদ পাইবার সুযোগ পাইয়া থাকিয়া গেলাম।
কয়েক দিনের মধ্যেই দেখিলাম নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের উপর আমার ছায়া পড়িয়াছে। ছায়া আমি ফেলিয়াছি। তুমি আমাকে স্বর্ণলতার কাছে সেই ধাঁধা প্রেরণ করিবার জন্য দ্বিপ্রহরে তোমার ঘরে আহ্বান করিলে। আমি মনে মনে হাস্য করিলাম; উৎসাহিত হইলাম। তাহার পর তোমার বিবাহ হইল। তোমার মাতাপিতার সঙ্গে আমার চলিয়া যাইবার কথা। আমি সরস্বতী বউকে ধরিলাম; বলিলাম—ভাই বউ, জ্যাঠাইমা জ্যাঠামশাইয়ের নিকট কোন প্রবীণাকে পাঠাইয়া দাও। আমি ভাই তোমাদের যুগলের আশ্রয়ে থাকিয়া জীবন সার্থক করিব। তোমরা শয়ন করিবে, আমি শয্যা রচনা করিব, আমি তোমাকে কেমন করিয়া পুরুষের নাসিকা কুঁড়িয়া দড়ি পড়াইতে হয় শিখাইব। পান সাজিব। এবম্বিধ নানাপ্রকার তোষামোদ করিয়া তাহাকে দিয়াই তোমাকে বলাইলাম। জ্যাঠাইমাকে বলাইলাম। সঙ্কল্প করিলাম, তোমাকে জয় করিব।
আমি বলিলাম—অঞ্জনা, তুমি থাম। তুমি থাম। এসব কথা বলিলে পাপ হয়, শুনিলে পাপ হয়—তুমি থাম।
অঞ্জনা বলিল-সে তোমার হয়, আমার হয় না। আমাদের মত যাহারা তাহাদের হয় না। যে ভগবান এবম্বিধ অদৃষ্ট দিয়া আমাদের জগতে পাঠান তিনি আমাদের এবম্বিধ চরিত্র দেন। আর তুমি এবং তোমার মত যাহারা শুদ্ধাচারী, তাহারা ভণ্ড, তাহারা কালী কালী হরি হরি জপ করিয়া দন্তে দত্ত টিপিয়া পড়িয়া থাকে, তুষানলে দগ্ধ হয়
সভয়ে আমি বলিলাম—অঞ্জনা!
অঞ্জনা বলিল-আমি তোমাকে জানি না মনে করিতেছ? তোমার প্রতি পদক্ষেপ আমি চিনি, তোমার মুখ দেখিয়া বলিতে পারি কী তুমি ভাবিতেছ। মুখ খুলিলে বলিতে পারি কি বলিবে। আমাকে দেখিলে তোমার দৃষ্টি উৎফুল্ল হয় না? আমি থাকিলে সরস্বতী বউয়ের সঙ্গে আলাপনের মধ্যে তোমার উচ্ছ্বাস বাড়ে না? কোনক্রমে আমার হাতে হাত ঠেকিলে তুমি চঞ্চল হও না? সত্য বলিবে!
আমি এবার কঠোর হইয়া বলিলাম-না-না-না!
অঞ্জনা কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর বিষণ্ণ থাকিয়া বলিল-তুমি মিথ্যা বলিলে।
আমি বলিলাম—না।
অঞ্জনা বলিল-তবে সত্য গোপন করিলে। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মত অশ্বত্থামা হতঃ ইতি গজের মতই কথাটা বলিলে। জমিদার হিসাবে তোমাকে লোকে ভয় করে। মানুষ হিসাবে তুমি আরো ভয়ঙ্কর। হাঁ, অস্বীকার করিব না তুমি অত্যন্ত সতর্ক। তুমি হাসিতে হাসিতে হঠাৎ গম্ভীর হইয়াছ। তোমাকে একাকী দেখিয়া তোমার ঘরে প্রবেশ করিলে তৎক্ষণাৎ তুমি কোন-প্রকার ছুতা করিয়া স্বর্ণলতাকে আহ্বান করিতে। বা চাকরকে আহ্বান করিতে! স্বর্ণলতার সম্মুখে তোমার উল্লাসে আমি পুলকিত হইতাম কিন্তু তোমাকে একাকী পাইয়া কাছে ছুটিয়া গিয়াও সভয়ে সরিয়া আসিতাম।
অতঃপর সহসা সে যাহা করিল তাহাতে আমি ভীত হইলাম, চঞ্চল হইলাম। সে কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল—কেন, আমাকে কি এতটুকু ভালবাসা তুমি দিতে পারিতে না? এতটুকু? এক কণা? স্বর্ণলতার উচ্ছিষ্ট এতটুকু? তাহাতেই আমি কৃতার্থ হইতাম। এই তো সারা দেশময় জমিদারদের দুইটা তিনটা করিয়া স্ত্রী থাকে। রক্ষিতা থাকে। বাড়ীতে আশ্রিতাদের মধ্যে কত সুন্দরী যুবতীকে তাঁহারা অনুগ্রহ করেন। তাহাতে কি ক্ষতি হয়?
—তাহা ছাড়া রত্নেশ্বর, স্বর্ণলতা তোমার যোগ্যই নয়। নামেই লেখাপড়া জানা সরস্বতী বউ। রঙটাই কটা। আমার সঙ্গে তাহার তুলনা! তুমি ভয়ঙ্কর বলিলাম, ভুল বলিলাম। তুমি কাপুরুষ। তুমি পুরুষই নও। তুমি সিংহ নও, তুমি শশক।
আমি কঠোর কণ্ঠে তাহাকে বলিলাম—তুমি দুশ্চরিত্রা! চুপ কর তুমি।
অঞ্জনা তাহাতেও দমিল না। সে বলিল—হাঁ, আমি দুশ্চরিত্রা। অন্তত মনে মনে আমি দুশ্চরিত্রা। তুমি সাধু। তুমি ভয়ঙ্কর। সেই প্রেতিনীর গল্প আছে—যাহারা সুযোগ পাইয়া সুন্দর পুরুষকে আশ্রয় করে, তাহাকে চুষিয়া খায়, আমি তাই। সেইরূপ ভাবেই তোমাকে চুষিয়া খাইবার জন্য তোমাকে আশ্রয় করিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু পারিলাম না। কাঁদিতে কাঁদিতে প্রহার খাইয়া আমাকে পলাইতে হইতেছে। কিন্তু তুমিও জ্বলিবে। নিশ্চয় জ্বলিবে। এই তেজ তোমার থাকিবে না।
আমি শিহরিয়া উঠিয়া বলিলাম- অঞ্জনা! অঞ্জনা–শোন।
সে চলিয়া যাইতেছিল, ফিরিয়া দাঁড়াইল। আমি তাহাকে বলিলাম- কদাচ এ কার্য করিও না। কদাচ না। তাহা হইলে আমি তোমাকে সত্যই হত্যা করিব।
সে কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর সে ফিরিয়া চলিয়া গেল। আমি বুঝিলাম এবার ঔষধ ধরিয়াছে। সে ভীত হইয়াছে এবং বুঝিয়াছে!”
সুরেশ্বর খাতাখানা বন্ধ করলে।
সুলতা বললে–অদ্ভুত মেয়ে।
সুরেশ্বর বললে—বল, কি বলবে এর সম্বন্ধে?
—ওর সম্বন্ধে বলব, হাসলে সুলতা, বলল —তুমি কি বলবে জানি না, আমি বলব- সে চেয়েছিল তার ন্যায্য প্রাপ্য। কিন্তু পায় নি।
—রত্নেশ্বরকে সে চেয়েছিল, কিন্তু রত্নেশ্বরের কি তার দাবী মেনে আত্মসমর্পণ করা উচিত ছিল?
—রত্নেশ্বর ছাড়াও আরো অনেক মানুষ ছিল, যারা রত্নেশ্বর থেকে কম উজ্জ্বল, কম গুণবান নয়। হয়তো ধনী না হতেও পারেন। সে স্বচ্ছন্দে ডাইভোর্স ক’রে তাদের একজনকে বিয়ে করে সুখী হতে পারত।
হেসে সুরেশ্বর বললে—তা সে করেছিল সুলতা। সে রত্নেশ্বর রায়ের সমস্ত শাসন, সমস্ত বন্ধন অস্বীকার ক’রে কলকাতায় জানবাজারের এই বাড়ী থেকে একদিন রাত্রে চলে গিয়েছিল। তখন কলকাতার বাড়ীতে রত্নেশ্বর রায় শিকারের জন্য একজন পোর্তুগীজ ফিরিঙ্গীকে রেখেছিলেন। ওই হ্যারিসের মতো চরিত্র। এবং আশ্রয় নিয়েছিল ক্রীশ্চান চার্চের। যেখানে রত্নেশ্বর রায়ের হাত পৌঁছায় না। যাবার সময় একখানা চিরকুট লিখে গিয়েছিল। “পাপ তোমার কাছে হারিয়া পলাইতেছে।”
সুরেশ্বর একটু থেমে কথার জের টেনে বললে—এই জন্যেই আমি রায়বাড়ীর পূর্বপুরুষের ব্যভিচার-সঙ্গিনী সেই যোগিনী মেয়েটার চেহারা অঞ্জনার চেহারার আভাস নিয়ে এঁকেছি। অঞ্জনাকে আমি অপমান করতে চাই নি। আমাকে তুমি ভুল বুঝো না।
আরো আছে সুলতা। অঞ্জনার কথাটা তুমি ক্ষুব্ধ হয়ে তুললে বলে ক্রমভঙ্গ করে বলতে হ’ল। এখন আমার জবানবন্দীর ক্রমে ফিরে চল। ১৮৫৯ সালে রত্নেশ্বর রায়ের বিবাহ হল। অঞ্জনাকে স্বর্ণলতাই চেয়ে নিলে শাশুড়ি ভবানী দেবীর কাছে।
শুধু বীরেশ্বর রায় একটু খুঁতখুঁত করছিলেন। বলেছিলেন—তাই তো!
সুরেশ্বর বললে—বীরেশ্বর রায় প্রস্তাবটা শুনে বলেছিলেন—তাই তো!
ভবানী বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন—কেন, তাই তো কেন বলছ!
—তোমার মনে হচ্ছে না? অঞ্জনা এখানে বউমার কাছে থাকবে বলছ?
—আমার কাছে থাকলে আমার সুবিধে হত। তোমার খাবার, সেবার ভারটা ওর উপর দিলে আমি নিশ্চিন্ত হতাম। অঞ্জনারও আমাদের সঙ্গে তীর্থদর্শন হত। কিন্তু বউমার কথাও তো ভাবতে হবে। বউমা বলছেন-ও থাকলে আমি কথা কইবার লোক পাব। ও ভারী মজার মজার কথা বলে। এত বড় বাড়ীতে-চুপ করলেন বউমা। তবে বুঝলাম। কথাটা তুমিও ভাবো, এত বড় বাড়ীতে ওই অল্পবয়সী মেয়ে, হাঁপিয়ে উঠবে যে।
বীরেশ্বর রায় বলেছিলেন—একবার রত্নেশ্বরকে ডেকে দিয়ো। তোমার সঙ্গে তার এ বিষয়ে কোন কথা হয়েছে?
ভবানী দেবী বলেছিলেন—তার সামনেই তো কথা হল। মায়ের মন্দির থেকে এলাম, বউমা, অঞ্জনাও আমার সঙ্গে ছিল। পূজার পর, ভোগের আগে বউমা বললে—আমার শরীরটা কেমন করছে মা। দেখলাম খুব ঘেমে গেছে। বললাম—তুমি চলে যাও, আমি রয়েছি; অঞ্জনা রয়েছে, তোমার চলে গেলে কোন দোষ হবে না। বউমা চলে এল নিজের ঝিকে নিয়ে। ফিরে এসে তোমায় মার চরণামৃত পুষ্প দিয়ে রত্নকে দিতে গেলাম, দেখলাম, বউমা একটু সুস্থ হয়েছেন, ছেলেমানুষ, সায়েবী চালে মানুষ, এসব অভ্যেস নেই। বললাম—এখন সুস্থ লাগছে তো?
রত্ন বলল—ওঃ, সে ঘেমে নেয়ে উঠেছিল যেন। এসে ধপ করে বিছানায় শুয়ে পড়ল। তারপর বললে—বাবাঃ, পেটের ভেতর আমার হাত-পা সেঁধিয়ে যাচ্ছে। ভয় করছে। এ সব আমি সামলাব কি করে? মা চলে যাবেন! বললাম-কিন্তু পারতে হবে। না পারলে তো চলবে না। তুমি নিজে চোখে বিয়ের আগে এসে সব দেখে গিয়েছ! তা সাহস আছে, বললে —পারব বই কি। এসব ভাল লাগছে খুব। কিন্তু কখনো তো করি নি। দেখে ভাল লেগেছিল। এখন সেই সব করতে গিয়ে খেই হারিয়ে যাচ্ছে। ভয় হচ্ছে। কোথায় খুঁত হচ্ছে, কোথায় খুঁত হচ্ছে!
হেসে ভবানী দেবী বলেছিলেন-এর পর যখন অভ্যেস হবে, তখন দেখবে, মা তোমাকে অনবরত হেসে বলছেন, ভয় কি? ভয় কি বেটী? ওরে আমি যে মা! আমার কাছে খুঁত হয় সন্তানের? তাছাড়া মাসিমা রইলেন, উনিই এতদিন করে আসছেন, তোমার হাতে-হাতে সব যুগিয়ে দেবেন; বলে দেবেন। ওই দেখ না, অঞ্জনা সব কেমন অবলীলাক্রমে করে যাচ্ছে। ভবানী বীরেশ্বর রায়কে বললেন—এই কথাতে রত্নেশ্বরই বললে-তোমার বউমা আমাকে একটা কথা বলছিল।
ভবানী দেবী বলেছিলেন—কি?
রত্নেশ্বর বলেছিলেন স্বর্ণলতাকে বল না, তুমি নিজেই বল না। আমাকে বললে কি হবে? খোদ মাকে বল। আমি বলতে পারব না।
—কি বউমা?
স্বর্ণলতা শাশুড়ির সামনে ঘোমটা টেনে বসেছিলেন। রত্নেশ্বর বলেছিলেন-আমি বাইরে যাচ্ছি। তুমি শোন, ও কি বলছে।
তখনকার কালে বউ শাশুড়ির সামনেও ঘোমটা দিত, এবং চাপা গলায় কথা বলত। অবশ্য ঘোমটা সারা-মুখ-ঢাকা ঘোমটা নয়, কপাল ঢেকে অন্তত ইঞ্চি দুই সামনের দিকে ঝুলে থাকত।
মৃদু কণ্ঠে স্বর্ণলতা বলেছিলেন- বলছিলাম, অঞ্জনা ঠাকুরঝির কথা!
—কি কথা? অঞ্জনা কিছু বলেছে বুঝি?
—না, ঘাড় নেড়ে ইঙ্গিতে কথাটা সেরেছিলেন নবীনা রায়বধূ।
এবার রত্নেশ্বর ভিতরে ঢুকে এগিয়ে এসেছিলেন এবং বলেছিলেন—মা তো আমার বাঘিনী বউ-কাঁটকী শাশুড়ি নয়। বলতে গলা শুকুচ্ছে! ও বলছিল, তুমি চলে যাবে, একলা হবে ও; এইসব দেবতার কাজ; ঠাকুমা বলতে গেলে বুড়ী হয়েছেন। এই তো বিয়েতে খেটে নেচে খেয়ে আজ প্রায় মাসের উপর পড়ে আছেন। সেরে গেছেন, তবু উঠতে পারেন না। তার ওপর বাতের ব্যথা। আর ওঁর কথাবার্তা বড় সেকেলে। শুধু সেকেলে নয়, একটু চ্যাটাং-চ্যাটাং। তোমাকেই কি বলেছিলেন, তোমার মনে আছে। তাই বলছিল, অঞ্জনা যদি ওর কাছে থাকত, তো ভাল হত। বলছিল—ঠাকুরঝি যদি এখানে থাকত তাহলে খুব ভাল হত। সব কাজ দিব্যি করা যেত দুজনে মিলে, হাসি-গল্পের মধ্যে। এই আর কি। কি বল না। ঘোমটাসুদ্ধ ঘাড়টা নেড়েও তো জানাতে পার!
তাই জানিয়েছিলেন নতুন বউ।
ভবানী দেবী হেসে বলেছিলেন-তোমার আমার কথা ছিল আলাদা। শাশুড়ি ছিলেন না। শ্বশুর ছিলেন, তিনি থাকতেন কীর্তিহাটে তো তুমি আমায় নিয়ে ছুটতে কলকাতায়। আবার তিনি কলকাতায় গেলে তুমি আমায় টেনে আনতে এখানে। ঘোমটা দিতে হত না। সমীহ করবার কেউ ছিলেন না। তার ওপর সে আমলে ঘোরতর সাহেব তুমি।
বীরেশ্বর বলেছিলেন- হুঁ। শুধু একটা হুঁ।
ভবানী দেবীর খেয়াল হয়েছিল, এতক্ষণে, তিনি বলেছিলেন—তুমি কি ভাবছ বল তো!
—ভাবছি, তাহ’লে অঞ্জনার স্বামীকেও এখানে রাখতে হবে।
—তা তো কথাই হয়েছে।
—না, এই বাড়িতেই, তার জন্য নিচের তলায় সংসার পাতিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করতে হবে। লোকটা মদ খায়, যাত্রা করে বেড়ায়, বাউন্ডুলে। তাহলেও অন্দরেই তাকে থাকতে দিতে হবে।
—কেন? তা করতে হবে কেন? সে তো অঞ্জনাকে নেয় না। গণ্ডা দরুণে বিয়ে। চাকরি অঞ্জনার খাতিরে দিতে আমরা চাচ্ছি, কিন্তু অঞ্জনা বলছিল, কেন মিথ্যে তাকে চাকরি দেবেন জ্যাঠাইমা, সে চাকরি করবার মানুষ! দুদিন পর পালিয়ে যাবে। না হয় কারুর সঙ্গে মারপিট করবে। না হয় মাতলামি করে, আমার লজ্জার আর শেষ রাখবে না। আমাকে দয়া করে কাছে রাখবেন, এতেই আমি বাঁচলাম। এই ঢের। সংসার আমার অদৃষ্টে নেই। আর ও আমি চাইনে। ও কাজ করবেন না। আমি বললাম—দেখি না! তখন বললে—দেখুন! আপনাদের কাছে আমার অপমান নেই; আর সবই বলে রাখছি যখন, তখন আমাকে এর জন্য দায়ীও করবেন না, আপনারা। এর পর চাকরি দেবো বলেছি দেব, কিন্তু বাড়ীতে তাকে ঢুকতে দেবো কেন?
—তাহলে অঞ্জনার জন্যে আলাদা বাড়ী করে দিতে হবে।
—আলাদা বাড়িতেই যদি থাকবে, তাহলে এ বাড়ীর ওইসব কাজ চব্বিশ ঘণ্টার কাজ তা হবে কি করে? ধর ভোররাত্রে মঙ্গল আরতি। শয়ন হয় রাত্রি এক প্রহরের পর। তখন শয্যাভোগ দেওয়া, তারপর বাড়ীর খাওয়া-দাওয়া, কারুর অসুখ থাকলে তাকে একবার দেখা।
বাধা দিয়ে বীরেশ্বর বলেছিলেন—তোমাকে কি বলব, বুঝতে পারছি না আমি। আমাকে দেখেও তুমি পুরুষ-চরিত্র বুঝলে না ভবানী! পুরুষের মন বহুগামী। তোমার দাদা বিমলাকান্ত দু-চারটেই হয়। তার বেশি হয় না। তার উপর ভূস্বামী, বলতে গেলে রাজা।
—ছিঃ! বলে উঠেছিলেন ভবানী। তুমি নিজে নিজের মুখে কালি মাখাচ্ছ, মাখাও। জোর করে মাখাচ্ছ। কিন্তু আমি তো জানি। সোফিয়াকে নিয়ে—। থাক ওসব কথা। নিজের ছেলেকে এত ছোট ভেবো না।
বীরেশ্বর বলেছিলেন—ছোট আমি নিজেকে ভাবিনে কোনোদিন। তবে ভয় আমার ওই অভিসম্পাতের, তোমার বাবা—
শিউরে উঠে ভবানী দেবী বলেছিলেন—না। আমি তার জন্য সাধনা করেছি, না তা হবে না।
বীরেশ্বর হেসেছিলেন, বলেছিলেন—ভাল।
কথাগুলো আড়াল থেকে শুনেছিলেন রত্নেশ্বর রায়। এবং নিঃশব্দে ফিরে এসেছিলেন। বাপের উপর ক্রোধ হয়েছিল তাঁর!
তিনি ডায়রীতে লিখেছেন—“পিতার বাক্যগুলি অন্তরাল হইতে শ্রবণ করিয়া আশ্চর্যান্বিত হই নাই। সারাটা জীবনই তিনি অকারণে সকলকে সন্দেহ করিয়া গেলেন। আমার মাতৃদেবী যিনি সাক্ষাৎ দেবী, সারাটা জীবন যিনি তপস্বিনী, তাঁহাকে সন্দেহ করিয়াছিলেন। আমার সাধুপ্রকৃতির চরিত্রবান মাতুলকে সন্দেহ করিয়াছিলেন। তিনি আমার উপর সন্দেহের আশঙ্কা পোষণ করিবেন ইহাতে আশ্চর্যের কি আছে? তথাপি ইহা শ্রবণ করিয়া আমার কর্ণকুহর যেন দগ্ধ হইয়া গেল। যিনি সারাটা জীবন একজন বাঈজীকে লইয়া প্রমত্ত থাকিলেন, কি বলিব, অন্তরে অন্তরে সময়ে সময়ে দাবানল সদৃশ অনলজ্বালা অনুভব করিয়া থাকি, যখন মনে পড়ে সোফিয়া বাঈয়ের মোহ আজও তাঁহার অন্তরে ঘৃতলোভী অগ্নিশিখার মত জ্বলিতেছে। সোফি বাঈয়ের পরিবর্তন হইয়াছে অনেক। তাহার চরিত্রের বরং প্রশংসা করি, মদীয় পিতাকে সে প্রায় স্বামী জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে সঙ্গীতলহরী শুনাইয়া তৃপ্তি দান করে, উত্তম পান সাজিয়া দেয়। তাহাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু পিতাকে কি বলিব? এমত চরিত্র ব্যক্তি, এমত সন্দেহ করিবেন তাহাতে আশ্চর্য কি? তবে আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি আমার চরিত্রবল তাঁহাকে এবং সকল জগৎসমক্ষে প্রমাণিত করিব। এই অভিসম্পাতকে আমি ব্যর্থ করিব। পাপ মাত্রেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে। আমি প্রায়শ্চিত্ত করিব।
“অঞ্জনা সরস্বতী বধুর নিকটেই থাকিবে। এই বাড়ীতেই থাকিবে। এবং চব্বিশ ঘণ্টাই থাকিবে। রাখিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম।”
তাই রেখেছিলেন রত্নেশ্বর। অঞ্জনা স্বর্ণলতার কাছেই রইল। আরো মাসতিনেক পর কালীপুজোর পর বীরেশ্বর রায় গিয়েছিলেন কলকাতা। সকলেই তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন। রত্নেশ্বর, স্বর্ণলতা এমন কি অঞ্জনা পর্যন্ত
রত্নেশ্বর বীরেশ্বরের জন্যে খুব এলাহি ব্যবস্থা করেছিলেন। মহিন্দরী চাকর যেমন ছিল, তেমনি ছিল তামাক সাজা, কাপড় কোঁচানো, তেল মাখানো, গা-হাত-পা টেপা, সামনে হাজির থাকা ও তাঁর ওষুধ-পত্র ঠিক ঠিক সময়ে দেবার জন্য সেকালের কম্পাউন্ডারী জানা একজন লোক নিযুক্ত করেছিলেন; বীরেশ্বরের খাবার ভার ভবানী দেবীর উপর; সোফিয়া তাকে গান শোনাবে। পান সেজে দেবে। আর ভবানী দেবীর পরিচারিকা ছিলেন দুজন। একজন ব্রাহ্মণ-কন্যা, প্রৌঢ়া বিধবা। আর একজন কলকাতার বড়লোকের বাড়ীর উপযুক্ত একটি ঝি। এ ঝি খুঁজে দিয়েছিলেন কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়ীর জ্যাঠাইমা জগদ্ধাত্রী দেবী।
রত্নেশ্বর রায় কলকাতায় এসে প্রায় মাস দুয়েক থেকে ফিরেছিলেন কীর্তিহাটে। কার্তিকের মাঝামাঝি এসে ফিরেছিলেন পৌষের দশ তারিখে।
পৌষ মাসে কিস্তি আসছে, বাংলাদেশের জমিদারদের পৌষ থেকে চৈত্র চারটে মাস সমারোহের মাস। জমিদারী সেরেস্তায় যত কাজ হয়, তার বারো আনা কাজ এই চারটে মাসে। গ্রামে গ্রামে প্রজাদের খামারে ধান উঠছে। ধান ঝাড়াই হচ্ছে। পৌষ থেকেই আলু। আখ মাড়াইয়ের মরসুম মাঘ থেকে। তার সঙ্গে ছোলা মসুর-গম, নানান রবি ফসল। চৈত্রে তিল। এই কটা মাসেই জমিদারীর খাতায় জমার অঙ্ক হাজারে হাজারে। মহলে মহলে গোমস্তা সেরেস্তা পেতে বসেই থাকবে। পাইকেরা নিত্য প্রজার দরজায় দরজায় তাগিদ দিয়ে ফিরবে।
জমিদারবাড়ির লক্ষ্মীর ঘরে বড় চৌকো ত্রিশ-চল্লিশ মণ ভারী আয়রন চেস্টগুলো প্রায় নিত্যই খোলা হবে একবার করে। তাতে টাকা পড়বে ঝঙ্কার তুলে। জমিদারের কাছারী চলবে, সকাল থেকে বেলা একটা পর্যন্ত, আবার সন্ধের পর থেকে। দশটা বারোটা যেদিন যেমন। আটটার পর থেকে অবশ্য সেরেস্তায় কর্মচারীরা কলম পেষে, জমিদার বসেন তাঁর আসর-ঘরে।
শতরঞ্চের উপর সাদা ধবধবে চাদর; তার উপর পুরু দামী গালিচা, চারিপাশে বড় বড় তাকিয়া। রূপোর আলবোলা, তাওয়া দেওয়া কল্কে; রূপো-বাঁধানো হুঁকো, হুঁকোদানের উপর বসানো থাকে।
গ্রামের যাঁরা ওরই মধ্যে সম্ভ্রান্ত, তাঁরা আসেন। নানান আলোচনা হয়। বেশীর ভাগ গ্রামের সমাজ নিয়ে। কোনোদিন খোশ-গল্প হয়। উচ্চ হাসিতে সব গমগম করে ওঠে
কোনকোন দিন গানের মজলিশ বসে। মধ্যে মধ্যে ওস্তাদ এসে হাজির হন। মাঘ মাসের সারা মাসটা মায়ের সামনে নাটমন্দিরে ভাগবত পাঠ হয়। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতারা এসে গোটা নাটমন্দিরটা ভরিয়ে দিয়ে বসে।
সুরেশ্বর বললে—কীর্তিহাট যদি কখনো অচির ভবিষ্যতের মধ্যে যাও সুলতা, তাহলে তোমাকে নাটমন্দিরটা দেখিয়ে খুশী হই, তুমিও খুশী হও, তা বলতে পারি। মনে পড়ে গেল বলে, না বলে পারলাম না। প্রকাণ্ড নাটমন্দিরটার চারদিক ভাগ করা ছিল আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে। কালীমন্দিরের বিরাট বারান্দাটায় বসত ভদ্রঘরের মেয়েরা, তারা বর্ণেও উঁচু। এক পাশটা ব্রাহ্মণ, অন্য পাশটায় বৈদ্য-কায়স্থ থেকে অন্যেরা। চার-পাঁচটা বারান্দা বরাবর লম্বা সিঁড়ি আছে পর পর, গ্যালারির মত, সেখান পর্যন্ত। তারপর একটা রেলিং, তার এধারে পুরুষ-মহল, সেও ভদ্র উচ্চবর্ণ। আর তিন দিকটায় যাদের এখন নাম হয়েছে হরিজন, তারা এবং মুসলমান, কৃশ্চান।
সুলতা বললে—ক্রীশ্চান?
সুরেশ্বর বললে—গোয়ানদের ভুলে যাচ্ছ। ওই হিলডা বুড়ীর পাড়ার লোক।
—এরা ভাগবত শুনতে আসত?
—না, ভাগবত শুনতে আসত না; যাত্রা হলে শুনতে আসত, বাঈ নাচ, খেমটা নাচ হলে
আসত। আর আসত গল্প শুনতে।
বিস্মিত হয়ে সুলতা বললে-গল্প শুনতে?
—হ্যাঁ সুলতা, গল্প শুনতে। ভাগবত-কথকের মত সেকালে গল্প-কথক ছিলেন, যিনি গল্প বলতে আসর পাতলে পনেরো দিন পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতেন একটি গল্প।
—বল কি!
—হ্যাঁ। এঁদের বোধহয় শেষজনকে আমার দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি পাঁচদিন গল্প বলেছিলেন। এই কীর্তিহাটের ছবির কড়চায় একটা বিশেষ ছবি। গল্পগুলো বেতাল পঞ্চবিংশতি বা কথা-সরিৎসাগরের মত। একটা গল্প শুরু করে, তার থেকে ফ্যাকড়া বের করতেন, পাঁচ-ছয়-সাত থেকে পনেরো পর্যন্ত, তারপর শেষ দিনে প্রথম গল্প শেষ হত। কিন্তু সে থাক, এখন ১৮৬০ সালে ফিরে চল। ১৮৫৯ সালের নভেম্বরের প্রথমেই বীরেশ্বর রায় কীর্তিহাট থেকে গেলেন কলকাতা; ব্যবস্থা হল, সদলে যাবেন তীর্থদর্শনে, চাকর, ঠাকুর, ঝি, সরকার নিয়ে ভবানী দেবী এবং তিনি ঘুরতে যাবেন তীর্থ; তখন রেললাইন বসে গেছে মোটামুটি। যেখানে হয়নি সেসব জায়গায় নৌকো কিংবা পাল্কী বয়েল গাড়ী নিয়ে ঘুরবেন। সোফিয়া বাঈসুদ্ধ সঙ্গে গিয়েছিলেন, তিনি দিল্লীতে নিজামউদ্দিন আউলিয়ার দরগায় তসলিম রাখবেন, আজমীঢ় শরীফ যাবেন।
মনে তাঁর ইচ্ছে আজমীঢ় শরীফ থেকে আর ফিরবেন না।
রত্নেশ্বর রায় ফিরেছিলেন পৌষের দশ তারিখে, ইংরিজী ১৮৫৯ সালের ২৬শে ডিসেম্বর। তিনি অগ্রহায়ণের শেষে ফিরতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিয়ের পর সস্ত্রীক প্রথম কলকাতায় গিয়ে কলকাতার বড় বড় বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেয়েছিলেন। কারণ বীরেশ্বর রায় কলকাতায় এসে ছেলের বিয়ে উপলক্ষে বড় বড় বাড়ীর যাঁদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, নিমন্ত্রণপত্র চলত, তাঁদের নিমন্ত্রণ করে একটা বউভাত করেছিলেন; যার খরচ আট হাজার টাকা হয়েছিল। খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে নৃত্য-গীতও ছিল, একথা সহজেই অনুমান করতে পার। এর পর বড় বড় বাড়ী থেকে নিমন্ত্রণ আসতে শুরু করেছিল এ-বাড়িতে, বর-বধুর। অনেক বাড়ীতে সপরিবারে নিমন্ত্রণ। শুরু হয়েছিল জোড়াসাঁকোর জগদ্ধাত্রী দেবীর বাড়ী থেকে। রাণী রাসমণির বাড়ী থেকে উপঢৌকন এসেছিল। ও-বাড়িতে বীরেশ্বর রায় সস্ত্রীক পুত্র পুত্রবধূ নিয়ে রানীকে দেখাতে গিয়েছিলেন। জানবাজারের বাড়ীর জমি দানের জন্যও বটে, আর রাণীর মহিমাময়ী চরিত্রের জন্যও বটে, তাঁর উপর বীরেশ্বর রায়ের শ্রদ্ধা ছিল অগাধ।
এর মধ্যে আবার নতুন জুড়ি কেনা হয়েছিল। এবার কালো ঘোড়া নয়, সাদা একজোড়া ওয়েলার, দাম দেড় হাজার টাকা এবং গাড়ীটা ল্যান্ডো। সেই গাড়ীতে চড়ে রত্নেশ্বর কলকাতায় দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে বেড়িয়েছিলেন। কলকাতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় তখনো পর্যন্ত অল্প। ছেলেবেলা বালক বয়সে বিমলাকান্তের সঙ্গে এসে বছর খানেক কি তার কম কলকাতায় ছিলেন। তারপর চলে গিয়েছিলেন কাশী। ফিরেছিলেন দীর্ঘকাল পর; তখন তিনি যুবা। অনেক কাণ্ডের পর বাপের সঙ্গে পরিচয় এবং পুনর্মিলনের পর রুগ্ন বীরেশ্বরকে নিয়ে কলকাতায় এসে মাস চারেক ছিলেন, কিন্তু তার মধ্যে পুরো এক মাস তাঁকে জামিনে খালাস থাকতে হয়েছিল। সে সময় তিনি বের হন নি। এবার স্ত্রীকে নিয়ে নতুন ল্যান্ডো গাড়ীতে, নতুন সাদা জোড়া ঘোড়ায় জৌলুস ছড়িয়ে বের হতেন। কালীঘাট থেকে দক্ষিণেশ্বর এবং স্ট্র্যান্ডরোডের গঙ্গার ধার থেকে, লাটসাহেবের বাড়ির চারদিক থেকে সিঁথিতে এখন যেটাকে চিড়িয়ার মোড় বলে সেখানে কোন সাহেবের চিড়িয়াখানা পর্যন্ত ঘুরে দেখেছিলেন সেবার। তাঁদের সঙ্গে থাকত অঞ্জনা। তার কাছে থাকত খাবারের কৌটো, জলের কুঁজো, পানের বাটা, কোচ বক্সে কোচম্যানের পাশে মহাবীর সিং দারোয়ান, তার কোমরে সরকারী লাইসেন্সে বলীয়ান তলোয়ার। পিছনে জোড়া-পোশাক পরা সহিস।
তখন কলকাতায় নতুন যুগ। ১৮৫৭ সালের মিউটিনির পর থেকে ইংরেজের প্রতাপে কলকাতা, যে বনে বাঘ থাকে সেই বনের মত হয়ে অন্য জন্তুর উপদ্রব থেকে শান্ত হয়েছে।
তুমি হয়তো জান, তবুও পুরনো কলকাতার কথা আমার কড়চায় আছে বলেই বলছি, পুরনো কলকাতা ১৮৫৭ সালের আগে খুব শান্ত ছিল না। হুতুমের নক্শায় এর পরিচয় আছে। মেলায়, খেলায়, পথে-ঘাটে ১৮৫৭ সালের আগে নানান উপদ্রব ছিল। সমাচার দর্পণে ১৮৪০ সালের একটা খবরের কথা রত্নেশ্বর রায় তাঁর ডায়রীতে লিখেছেন এই প্রসঙ্গে। বারোয়ারীর পাণ্ডারা নানান অত্যাচার করত। বিশেষ করে সঙ্গে স্ত্রীলোক থাকলে লাঞ্ছনার সীমা থাকত না।
দর্পণের খবরটা বেহালা সম্পর্কে। সেটা এই—“মান্য সাবর্ণ মহাশয়দিগের যুবা সন্তানেরা বারোয়ারি পূজার নিমিত্ত অনেক লোকের উপর অত্যাচার করিতেছিলেন। স্ত্রীলোকের ভুলি পাল্কি দৃষ্টিমাত্রেই বারোয়ারীর দল একত্র হইয়া তৎক্ষণাৎ আটক করিতেন এবং তাহাদিগের ইচ্ছামত প্রণামী না পাইলে কদাপি ছাড়িয়া দিতেন না। স্ত্রীলোকদিগের সাক্ষাতে অবাক্য উচ্চবাচ্য যাহা মুখে আসিত, তাহাই কহিতেন, তাহাতে লজ্জাশীলা কুলবালা সকল টাকা-পয়সা সঙ্গে না থাকিলে বস্ত্রালঙ্কারাদি প্রদান করিয়া মুক্ত হইতেন।”
সুলতা বললে—মনে পড়েছে, পেটন সাহেব নামে একজন দুদে ম্যাজিস্ট্রেট মেয়ে সেজে পালকি চড়ে বেহালায় এসেছিলেন। এরা জবরদস্তি করে পালকির দরজা খুলতেই সাদা গোখরোর মতো বেরিয়েছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট পেটন
—হ্যাঁ। পেটন সাহেব সেবার শায়েস্তা করলেও পুরো শায়েস্তা হয় নি। হুতোমের কালীপ্রসন্ন সিংয়ের জন্ম ১৮৪১ সালে, তাঁর নকশায় আছে, তাঁর আমলে একবার এক বারোয়ারীতলার প্রতিমার সিংহ ভেঙেছিল আনবার সময়। সেই সিংহ মেরামতির জন্যে টাকা চাই। তারা পরামর্শ করে আটকেছিল এক বিশিষ্ট সিঙ্গি মশায়কে। চাকুরে মানুষ। আপিস যাবেন। তাঁকে পথে আটকে ধরেছিল মায়ের সিঙ্গির পা ভেঙেছে, এখন সিঙ্গি কোথায় পাই, আমাদের উপর স্বপ্ন হয়েছে, আপনাকে এনে বসাতে হবে, মা দুর্গার পায়ের তলায়। সিঙ্গি মশায় মেরামতি খরচ দশ টাকা জরিমানা দিয়ে রেহাই নিয়েছিলেন।
কিন্তু ১৮৫৭ সালে মিউটিনি দমনের পর ইংলন্ডেশ্বরী যখন ভারতেশ্বরী হলেন, তখন কলকাতার ওই হাল পাল্টাল। ইংরেজের ভয়ে তখন ফণা গুটিয়ে গর্তে ঢুকেছে সব।
তবু রত্নেশ্বর রায় দারোয়ান ছাড়া যেতেন না কোথাও। প্রয়োজন হলে একজনের জায়গায় দুজন নিতেন।
ডায়রীতে লিখেছেন—“দারোয়ান ইত্যাদি লইয়া অদ্য চিড়িয়াখানা দেখিয়া আসিলাম। দুইজন দারোয়ান লইয়াছিলাম। কলিকাতায় এক শ্রেণীর ইতর গুণ্ডা ও উচ্ছৃঙ্খল ভদ্র যুবকের কথা শুনিয়াছি। আমি নিজেও সবল শক্তিমান। কাশীতে থাকিয়া কুস্তি করিয়া দেহ পাকাইয়াছি। কিন্তু কোন প্রকার উপদ্রব হয় নাই। সকল জীবজন্তু দেখিয়া নিরাপদে ফিরিলাম। অদ্যকার এই ভ্রমণ বড়ই আনন্দসহকারে উপভোগ করিয়াছি। একটি দৃশ্য দর্শন করিয়া চিত্তে রোমাঞ্চকর ভাবের উদয় হইল। এক জোড়া সবল ব্যাঘ্র ও ব্যাঘ্রীর প্রেমলীলা দেখিলাম, ব্যাঘ্রটি ব্যাঘ্রীকে কামড়াইতেছে, ব্যাঘ্রী তাহাকে থাবা মারিয়া প্রতিহত করিয়া গর্জন করিয়া যেন শাসন করিয়া কহিতেছে, নির্লজ্জ পুরুষ কোথাকার, তোমার কি কোনপ্রকার লজ্জাশরম নাই। এই এত লোকজনের সম্মুখে এসব কী হইতেছে।
আমার পার্শ্বেই স্বর্ণলতা অবাক হইয়া দেখিতেছিল। তাহার দিকে তাকাইয়া আমি সপ্ৰেম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। সে লজ্জায় মুখ নত করিল। আমি অগ্রসর হইয়া তদীয় হস্ত ধারণ করিয়া মৃদুস্বরে কহিলাম, দেখিতেছ!
সে বলিল —আঃ!
পিছন হইতে খুক খুক শব্দে কেহ হাস্য করিল। আমি মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম অঞ্জনা হাস্য করিতেছে। সে সব লক্ষ্য করিয়াছে।”
গাড়িতেও সামনের সিটে বসে অঞ্জনা বার বার মুচকে মুচকে হাসছিল। স্বর্ণলতা দেবী রাঙা হয়ে উঠেছিলেন। অঞ্জনা বলেছিল—এই আমি মুখ ফিরিয়ে উল্টো মুখে বসছি ভাই বউ। তাছাড়া ননদের আড়ি পেতে শোনা চিরকালের অভ্যাস। ওরা দেখলেও দোষ নেই, শুনলেও দোষ নেই। ছোটদাদা আমার চকোরের মত চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে। তুমি ভাই চাঁদ, মেঘের আড়ালের মত ঘোমটাটা সরাও।
সে সত্যিই মুখ ফিরিয়ে বসেছিল।
স্বর্ণলতা সুযোগ পেয়ে রোষকটাক্ষে শাসন করেছিল রত্নেশ্বরকে। রত্নেশ্বর সেই গাড়ীর মধ্যেই হা-হা শব্দে হেসে উঠেছিলেন।
অঞ্জনা মুখ ফিরিয়ে বলেছিল- লজ্জা ভাঙল?
রত্নেশ্বর বলেছিলেন—অঞ্জনা, ঠিক বাঘিনীর মত তাকালে রে, হাতে আমার আবার চিমটি কাটলে।
অঞ্জনাও খিলখিল করে হেসেছিল। এবার স্বর্ণলতাও খুক খুক করে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসতে আরম্ভ করেছিলেন।
বাড়ীতে এসেই দেখেছিলেন, কীর্তিহাটের খবর এসেছে। সেখানে ফিরতে হবে। সামনে বড়দিন। ভেটের ব্যবস্থা যাবে কলকাতা থেকে। তার কেনাকাটা আছে। এবং ছোট হুজুরকে যেতে হবে, মেদিনীপুরে সাহেবদের সঙ্গে দেখা করবেন তিনি। হুজুরের শ্বশুর বলে দিয়েছেন, রত্নেশ্বর যেন আসে। বেয়াই মশাইয়ের কাল গেছে। এখন জেলার কর্তাদের সঙ্গে দহরম-মহরমটাই সবথেকে বড় কথা। আগে যা হয়েছে হয়েছে, এখন নতুন কালে নতুন চাল।
তা ছাড়াও বড় খবর ছিল, এবার শ্যামনগরের দে-সরকার শ্যামনগর বিক্রি করতে রাজী হয়েছে। তারা একবার ছোট হুজুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কিছু কথাবার্তা বলতে চায়।
খবর নিয়ে যিনি এসেছিলেন, তিনি ঠাকুরদাস পাল। বিয়ে করে তিনি চলে গিয়েছিলেন শ্যামনগর। শ্যামনগর বিক্রীর চিঠি তিনি এনেছেন। তাঁর মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে।
সুলতা বললে-রত্নেশ্বর নিজের পতনের ব্যবস্থা নিজেই করেছিলেন। মানুষ তাই করে। তবে দোষ তিনি ষোল আনা অঞ্জনার ঘাড়েই চাপিয়ে গেছেন নিশ্চয়।
সুরেশ্বর বললে—বারো আনা তো বটেই। তবে নিজের ঘাড়ে চার আনা নিয়েছিলেন —সে তাঁর ডায়রীতে আছে। সে তোমাকে প’ড়ে খানিকটা শোনালাম। পরে আরো আছে। কিন্তু আমার ক্রম ভেঙো না। ক্রমানুসারে বলে যাই, বলতে দাও।
এই যে দীর্ঘ ইতিহাসটি বললাম—এটি কিন্তু সব জেনেছিলাম একদিনে।
১৯৩৭ সালের শেষ জানুয়ারী শীতের দিন, সকাল বেলাতেই পুলিশ এসে বিমলেশ্বরকাকাকে ধরে নিয়ে গেল; অর্চনাকে তিনি বাঁচিয়ে কোমরে দড়ি পরে হাতে হাতকড়ি পরে পুলিশের সঙ্গে গ্রাম ঘুরে দেখিয়ে গেলেন, রায়বংশের ঋণ তিনি শোধ করলেন। ঋণ শোধ করতে তাঁর বৈষ্ণব ধর্মকে তিনি বিক্রী করেছেন, যে সম্মানটুকু ছিল তা বিক্রী করেছেন—অনুতাপ করেন নি।
কাকীমা আমাকে ডেকে বলেছেন—এর শোধ নেবে, তুমি আমাকে কথা দাও ভাসুরপো!
আমি কথা দিয়েছি। অর্চনা ঘরের মধ্যে মুখ লুকিয়েছে। তার কথা বিমলেশ্বরকাকার স্ত্রী, তাঁর জা অর্থাৎ অর্চনার মায়ের কাছেও প্রকাশ করেন নি। তিনি বর্ধমানের উকীলের মেয়ে, তিনি আইন বোঝেন। এবং দেশের অবস্থাটাও বোঝেন।
বাড়ীতে ফিরে এসে আমি গোপাল সিংয়ের ইতিহাস সংগ্রহ করেছি রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রী থেকে। মাঝখানে গ্রামের লোকেরা এসেছেন। প্রত্যেকে সেদিন সহানুভূতি জানিয়ে গেছেন। দয়ালঠাকুরদা—উরুকাকা এসে চোখের জল ফেলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলে গেছেন—শোধ নিয়ো।
বৃদ্ধ রঙ্গলাল মণ্ডল নিজে আসতে পারেন নি, শরীর তাঁর ভেঙে গেছে। তিনি বাড়ী থেকে বের হতে পারেন না, ওই কংগ্রেসের মিটিং যা অতুলকাকার কাণ্ড, তার পর থেকে। রঙলাল মণ্ডলমশায় সভাপতি হয়েছিলেন। পুলিশ যখন লাঠি চালায়, তখন অতুলকাকা নিজের দেহ দিয়ে তাঁকে ঢেকে মাটিতে শুয়ে পড়েছিলেন, তবু আঘাত নিবারণ করতে পারেন নি। একটা লাঠির গুঁতো তাঁর কোমরে লেগে হাড় ভেঙে দিয়েছিল। তাঁকে অ্যারেস্ট ক’রে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে দিয়েছিল, সেরে ওঠার পর প্রায় অক্ষম দেখে এবং বয়স দেখে ছেড়ে দিয়েছিল পুলিশ। লোকে বলে—তাঁর হয়ে তাঁর উকিল ছেলে একটা বন্ড গোছের কিছু লিখে দিয়ে ছাড়িয়ে এনেছিল বাপকে অক্ষম রঙলাল বিছানায় শুয়ে থাকতেন আর ওই উকীল ছেলেকে গালাগাল দিতেন। তাঁর বড় ছেলে আমার কাছে এসেছিল। বলেছিল—আমাদের বাড়ীর সামনে বিমলবাবুকে কোমরে দড়ি বেঁধে পুলিশ নিয়ে গিয়ে ইচ্ছে করে কিছুক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। লেফট রাইট লেফট রাইট বলে চেঁচিয়ে কনস্টেবলগুলোকে দিয়ে পা ঠুকিয়েছে। বাবাকে অনেক কষ্টে সামলে রেখেছিলাম। তাঁকে তো দেখেছেন—খুব চেঁচান তিনি! এখনো হাউমাউ করে কাঁদছেন। আপনার কাছে পাঠালেন, বললেন—সুরেশ্বরবাবুকে বলগা গিয়ে, এর শোধ যেন তিনি নেন।
আমার মনেও ক্ষোভের অন্ত ছিল না। সেই ক্ষোভের বশেই ডায়রী পড়ছিলাম। বিচার করবার জন্য নয়; দেখছিলাম পূর্বকালের ঘটনার মধ্য থেকে কোথায়ও কোন ছিদ্রপথ পাওয়া যায় কিনা যার মধ্য দিয়ে আইনের দড়ি পরিয়ে শিবু সিং এবং তার বাপ হরি সিংকে বাঁধতে পারি। কিন্তু পড়তে পড়তে কাহিনীর মধ্যে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। যে তন্ময়তায় রত্নেশ্বর রায়ের পূর্বকথা শেষ করে তাঁর দিনলিপিতে এসে পরে পৌঁছুলাম রত্নেশ্বরের বিয়েতে, রায়বাড়ীর জীবন-নাটকে, অঞ্জনার প্রবেশে এবং বীরেশ্বর রায়ের প্রস্থানে।
সুলতা প্রশ্ন করলে—প্রস্থানে? মানে?
—তার অর্থ বীরেশ্বর রায় আর কীর্তিহাটে ফেরেন নি। ওই যে গেলেন তিনি কীর্তিহাট থেকে কলকাতা। এবং তারপর কলকাতা থেকে তীর্থে।
—তীর্থে মৃত্যু হয়েছিল তাঁর?
—না। বৈরাগী তিনি ছিলেন না। স্ত্রী ভবানী দেবীর জন্য দেবতার পুষ্প চরণোদক এও তিনি নিত্য খেতেন তাঁর হাতে, তাঁর জন্যেই তীর্থে ঘুরেছেন, দেবমন্দিরে গেছেন, দেখতে গেছেন নিজের আগ্রহে কিন্তু প্রণাম করেছেন স্ত্রীর ইচ্ছায়, নিজের ইচ্ছায় নয়। শুধু গয়াতে গিয়ে পিণ্ড দিয়েছিলেন নিজের আগ্রহে। থাক; এমনভাবে বলার থেকে গুছিয়ে বলি।
***