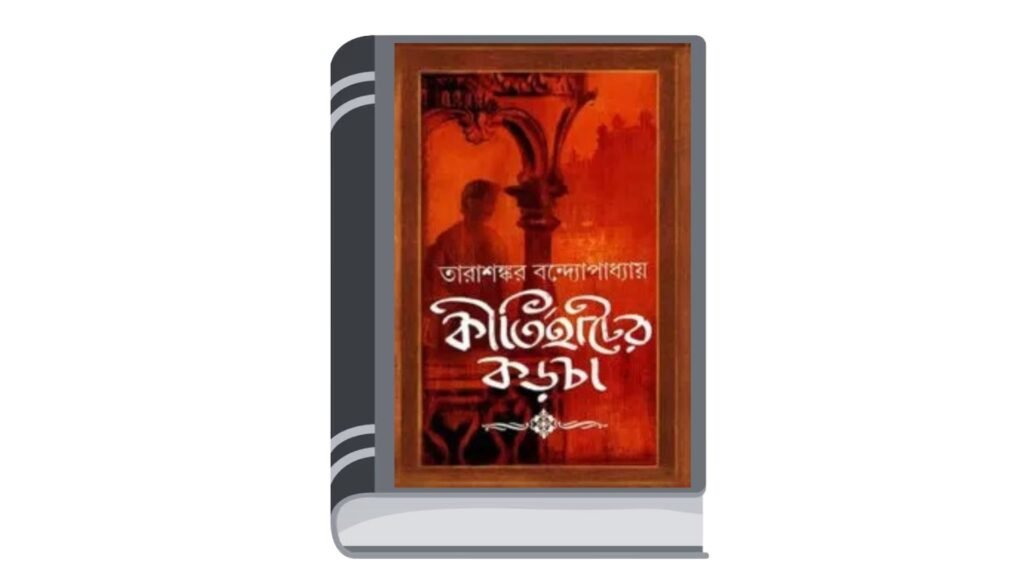কীর্তিহাটের কড়চা – ৩য় খণ্ড – ১৩
১৩
১৮৫৯ সালের ডিসেম্বরে বড়দিনের আগেই ফিরলেন তিনি। সরস্বতী বউয়ের বয়স তখন মাত্র চৌদ্দ। সুতরাং অঞ্জনার মত একটি চিত্তরঞ্জিনী চতুরা অতি সুকৌশলে তার মধ্যে নিজের ইচ্ছাগুলো সঞ্চারিত করে দিত।
রত্নেশ্বর রায় ডায়রীতে লিখেছেন—বিপদে পড়িলাম। কীর্তিহাট হইতে নায়েব এবং মেদিনীপুর হইতে পূজ্যপাদ শ্বশুর মহাশয় ওখানে যাইবার জন্য লিখিয়াছেন। গিরীন্দ্র আচার্য লিখিতেছেন- দে-সরকার শ্যামনগর বিক্রয় করিতে প্রস্তুত। এমন সময় স্বর্ণলতা সরস্বতী বউ একরূপ আবদার ধরিয়াছে কলিকাতায় বড়দিন না দেখিয়া যাইবে না। এখানে অবশ্য কলিকাতা দেখিয়া বেড়াইতেছি, আনন্দ করিতেছি, আমারও যৎপরোনাস্তি সুখ এবং আহ্লাদ হইতেছে। বিশেষ করিয়া পরিভ্রমণের সময়ে অঞ্জনা যেরূপ ননদোচিত হাস্যপরিহাসে আমাদের উভয়ের জীবনের আনন্দে চঞ্চল বায়ুপ্রবাহ হিল্লোলিত করিয়া তুলিতেছে তাহাতে সুখ ও আহ্লাদ যেন তরঙ্গিনীর তরঙ্গের ন্যায় নৃত্য করিয়া ছুটিতেছে। কিন্তু যে সব পত্রাদি পাইলাম তাহার পর আর কি করিয়া থাকা চলে? আমি সামান্য যুবক নহি; আমি কীর্তিহাটের রায়বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী। উত্তরাধিকারীই বা কেন, আমি অধীশ্বর। অদ্যই পিতা সকল পত্রাদি পাঠ করিয়া আমাকে ডাকিয়া কহিলেন।
বড়কর্তা বীরেশ্বর রায় বলেছিলেন—বস; যা পত্র এসেছে তাতে তোমাকে দু-তিন দিনের মধ্যে কীর্তিহাট ফিরতে হবে। জরুরি কাজ। বিশেষ ক’রে শ্যামনগর। শ্যামনগর ক্রয় সম্পর্কে যা পত্র দেখছি তাতে মনে হচ্ছে দে সরকাররা হয়তো বা কিছু কিছু সুবিধে চাইবেন। প্ৰতিশ্ৰুতি চাইবেন। হয়তো বা রাধানগর বাদ দিয়ে বাকী বিক্রী করতে চাইবেন। কিংবা ওঁদের সম্পত্তি জোতজমা নিষ্কর বলে স্বীকৃতি চাইবেন দলিলে। মৌখিক প্রতিশ্রুতিও কিছু চাইবেন বলে মনে হচ্ছে আমার। আচার্য হয়তো দিতে চাইছেন না—চাইবেন না। আমি বলব—দেবে। দেওয়া উচিত। তাঁরা নত হয়েই যখন চাচ্ছেন তখন দেবে। এগুলি হল রাজধর্ম। আমাদের দেশেও আছে, অন্যদেশেও আছে। আলেকজান্ডার পুরু রাজার সঙ্গে কি ব্যবহার করেছিলেন সে তো জান। আমাদের দেশে অজস্র আছে। শাস্ত্রেরও এই নির্দেশ। সুতরাং তাঁরা শ্যামনগর বিক্রী করছেন এইটেই আমাদের কাছে তাঁদের হার মানা। আমি হলে ওটা জলের দরে বিক্রী করে দিতাম, কিন্তু যার সঙ্গে ঝগড়া তাকে দিতাম না। অবশ্য—
একটু থেমে হেসে বলেছিলেন—অবশ্য ট্যারা দে-সরকার অর্থগৃধু অল্পপ্রাণী লোক; টাকাই তার কাছে সব। টাকা পেলে সে সব সইতে পারে, টাকার জন্যে সে সব করতে পারে। কিন্তু সে বিচার আমরা করব না।
রত্নেশ্বরের মন এতে সায় দিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন—আজ্ঞে হ্যাঁ। এতে সম্পূর্ণ একমত আমি। যা আদেশ করলেন তা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।
—হ্যাঁ। তবে শর্তগুলি যত্নসহকারে খুঁটিয়ে বুঝে দেখো। ওঁদের সম্পত্তি নিষ্কর এ আমরা দেব না। না। তা হতে পারে না। তা হ’লে প্রজা ঠিক হলেন না তাঁরা। মৌরসী ক’রে দিতে পার। খাজনা অন্তত বছরে একটা টাকাও দিতে হবে। বুঝেছ?
—আজ্ঞে বেশ। তাই হবে।
—আর একটা কথা।
—আজ্ঞা করুন।
—দেখ—। শুরু করেও চুপ ক’রে গিয়েছিলেন বীরেশ্বর।
কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে রত্নেশ্বর বলেছিলেন- বাবা!
—হ্যাঁ বলছি। আর একবার ভেবে নিলাম। ভেবে দেখলাম। দেখ—আমি মনে মনে অভিপ্রায় করেছি যে তুমি সম্পত্তির ছ আনার মালিক হয়েই আছো, বাকি দশ আনার মালিক এখনো আমি। তোমাকে আমার সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করেছি। তুমিই সব করছ। কিন্তু—।
চমকে উঠেছিলেন রত্নেশ্বর। কিন্তু পরমুহূর্তেই বীরেশ্বর রায় যে-কথা বলেছিলেন সে কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।
বীরেশ্বর রায় বলেছিলেন-দেখ আমি স্থির করেছি-অনেক চিন্তা করেই স্থির করেছি, যে আমার অংশ আমি দানপত্র করে তোমাকে দিয়ে আমি সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত হ’তে চাই।
বিস্ময়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে রত্নেশ্বর বলেছিলেন—কেন বাবা? আমার কি কোন ত্রুটি—না—না। তুমি আমার মুখোজ্জ্বলকারী পুত্র। তার জন্য নয়। কথা হল কি জান, এই যে কালটা এল, এটা সম্পূর্ণ নতুন কাল। এ কালের জমিদারী চালনা সে কালের প্রথায় চলবে না। জমিদারীকে যে অর্থে রাজত্ব বলতাম তা আর রইল না। ১৮৫৯ সালে যে নতুন প্রজাস্বত্ব আইন হল, সে আইনে জমিদারের আসল অধিকারই চলে গেল। কীর্তিহাটে যে আদেশ তুমি কাছারীতে জারী করেছ, তা খুব কালোচিত হয়েছে। প্রথমটা শুনে আমার ক্ষোভ হয়েছিল। পুত্র সকলেরই সমান রত্নেশ্বর, কিন্তু তুমি আমার কি তা অবশ্যই অনুমান করতে পার। সমুদ্রগর্ভে হারিয়ে যাওয়া নিধি। বিচিত্র কৃপায় ফিরে পেয়েছি তোমাকে।
রত্নেশ্বর ডায়রীতে লিখেছেন—“আমার মনে হইতেছিল আমি যেন স্থান কাল বিস্মৃত হইয়া যাইতেছি, ইচ্ছা হইতেছিল আমার এই হিমালয়তুল্য পিতৃদেবের চরণতলে লুটাইয়া পড়ি।”
বীরেশ্বর বলেছিলেন—মিথ্যা গোপন তোমাকে করব না। তোমার শ্বশুরমশায় কথাটা বলে গিয়েছিলেন—বেয়াইমশাই, কালটা বড় কঠিন পড়ল, আগের কাল গেল। কোম্পানী মানে বেনের দল আর দেশের মালিক রইল না, ব্রিটিশ ক্রাউন হল মালিক। এবার আর ঘুষের রাজত্ব রইল না। লাভের জন্য যা খুশী তাই করার কাল রইল না। এবার মহারানীর রাজত্ব, এ রাজত্বে বামুন চণ্ডাল জমিদার প্রজা ধনী দরিদ্র সব এক আইনের ফাঁদে বাঁধা পড়ল। নতুন অ্যাক্টটা পড়ে দেখুন। তখনো ঠিক আমলে আনি নি। তুমি শ্বশুরবাড়ী থেকে এসে নতুন হুকুম জারী করলে; শুনে একটু লাগল। আমার সঙ্গে পরামর্শ করলে না একবার? তারপর এখানে এসে অ্যাক্ট সম্বন্ধে আলোচনা হল কালীপ্রসন্ন সিংহীমশায়ের সঙ্গে, তিনিও বললেন-আরে মশাই, আগের কালে তলবমাত্রে প্রজার হাজিরানা ছিল কম্পালসারী। না এলে আপনি সিপাই পাঠিয়ে প্রজার ঘাড় ধরে আনতে পারতেন। আর তা পারবেন? অবিশ্যি রামাশ্যামাকে পারবেন। কিন্তু আমাকে পারবেন? আবার রামার পিছনে আমি দাঁড়ালে পারবেন? এ তো মশাই জুতো জামা পরা ঘোড়া হাতী চড়া গোমস্তাগিরি! জমিদারীর আর রইল কি? কথাটা ঠিক। আর ওতে আমার দরকার নেই রত্নেশ্বর। জমিদারী আমি তোমাকে দান করব। কলকাতার বাড়ী, আর নগদ টাকা আমার অংশের চার লক্ষের মধ্যে দু লক্ষ টাকা—এই আমার থাকবে। ওতেই আমি বেড়াব তীর্থ—নানা স্থান। বাস। পরমায়ু আমার বেশী দিন নেই। আমি বুঝতে পারছি। বাকী ক’টা দিন আনন্দ করে কাটিয়ে দেব। আমার অন্তে আমার উইল অনুযায়ী চাকরবাকরকে কাউকে পাঁচশো কাউকে হাজার কাউকে একশো দিয়ে যা থাকবে তার থেকে সোফিয়াকে পাঁচ বা দশ হাজার টাকা এবং জীবনস্বত্বে ওই এলিয়েট রোডের বাড়ী দেব। এবং অবশিষ্ট সবের মালিক হবেন তোমার গর্ভধারিণী।
স্তব্ধ হয়ে সব শুনেছিলেন রত্নেশ্বর।
বীরেশ্বর বলেছিলেন—তুমি আপত্তি করো না। এ তোমার জন্যেই করছিনে আমি। আমার জন্যই করছি—রায়বংশের জন্যই করছি। বুঝেছ। রায়বংশের জন্য। অবশ্য সোমেশ্বর রায়ের দেবোত্তরের বাইরের যা সম্পত্তি তাও আমি দেবোত্তর করে তোমাকেই তার সেবাইত করে দানপত্র করব। তুমি মালিক হবে সেবাইত সূত্রে। কোন শর্ত আমি আরোপ করব না। শুধু দেবত্র সম্পত্তি রইল দেবতার নামে। তাঁর সেবা চালিয়ে বক্রী আয় তুমি তোমার পছন্দমত খরচ করবে। আমি অপব্যয়ী। আমি বাল্যকাল থেকে ক্রোধীও বটে। এই গোমস্তাগিরির বড়লোকপনা এ আমার সইবে না।
সুরেশ্বর বললে—রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীতে একটি বিস্ময়কর কথা আছে, সুলতা, সেটি বলি, সেটি না বললে রায়বংশের জবানবন্দি কীর্তিহাটের কড়চা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সে কথা ভবানী দেবীর কথা
এই জানবাজারের বাড়ীর বড় হলঘরে কথাবার্তা হচ্ছিল পিতাপুত্রে। পাশের ঘরটা ছিল ভবানী দেবীর পূজার ঘর—নিজের ঘর। পাশেই ছিল ওঁদের শোবার ঘর। ওদিকের দক্ষিণ-পূব খোলা ওই ঘরখানা। ভবানী দেবী পূজায় বসে সব শুনেছিলেন। তিনি ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই ওঘর থেকে পূজার একটি জবাফুল এবং বিশ্বপত্র হাতে ক’রে এঘরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। পিতা পুত্র তাঁর দিকে তাকিয়ে চুপ করে গিয়েছিলেন। ঠিক গোপন করবার জন্য নয়। তাঁর উপস্থিতিতে ঠিক এই সব কথা যেন স্বচ্ছন্দে অসঙ্কোচে কওয়া যেত না।
রত্নেশ্বর তাঁর ডায়রীতে লিখেছেন—মাতৃদেবী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন আর তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করতঃ পিতৃদেব স্তব্ধ হইয়া গেলেন। আমিও তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলাম। এই পূজার পর তাঁহার যে মূর্তি হইত তাহা এক আশ্চর্য বিস্ময়জনক মূর্তি। মনে হইত তিনি যেন মানবী নহেন, কোন অপার্থিব দেবীমূর্তি। তিনি আসিয়া পিতার শয্যার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পিতৃদেব হস্ত প্রসারণ করিতেই তিনি পূজার জবাপুষ্প ও বিম্বদল তাঁহার হাতে তুলিয়া দিলেন। পিতৃদেব তাহা মস্তকে স্বহস্তে ধারণ করিয়া স্বকীয় উপাধানের তলদেশে রাখিলেন। অতঃপর মাতৃদেবী বামহস্তের রৌপ্যঘট হইতে কুশী করিয়া ইষ্টদেবীর চরণোদক তাঁহাকে পান করাইয়া কহিলেন- তুমি যাহা ধারণা করিয়াছ তাহা কদাপি ফলবতী হইবে না। বলিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন।
পিতা কহিলেন—কী মনস্থ করিয়াছি, কোন্ কথা বলিতেছ?
—তোমার উইলের কথা!
—হ্যাঁ। বলিতেছিলাম বটে। তুমি তা শুনিতে পাইয়াছ?
—পাইয়াছি। শুনিয়া মন চঞ্চল হইল। কিন্তু মা বলিলেন—চঞ্চল হইস না, ইহা কদাপি সত্য হইবে না।
পিতা ভ্রু-কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন- উইল করা হইয়া উঠিবে না?
—না, উইল তুমি করিবে। কিন্তু যাহা মনে করিতেছ তাহা হইবে না। তোমার পরিত্যক্ত সম্পত্তি এবং অর্থ ভোগ করিবার জন্য ভবানী কদাপি জীবিত রহিবে না। আমি অগ্রে যাইব। তুমি আমার বিরহে উন্মত্তবৎ হইবে। সতীহারা শিবের মত তোমাকে হাহাকার করিতে হইবে।
পিতৃদেব হাস্যকরতঃ বলিলেন—অতঃপর কি হইবে! তুমি উমা রূপে জন্মগ্রহণ করিবে এবং আমার তপস্যা ভঙ্গ করিয়া আবার আমার গৃহে আসিয়া আমাকে সংসারী করিবে!
মাতৃদেবীর অধরে শুক্লা দ্বিতীয়ার চন্দ্রমার মত ক্ষীণ হাসিরেখা ফুটিয়া উঠিল, তিনি কহিলেন-না। এতটা হইবে না। তবে তোমাকে। তিনি নীরব হইয়া গেলেন। অতঃপর একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করতঃ করিলেন—তাহা তোমাকে আমি বলিব না। অন্তত আজ বলিব না। আমি যেদিন যাইব সেইদিন বলিব। আমি শুধু বলিতেছি যে, তোমার উইলের মধ্যে আমার—নাম উল্লেখ করিয়া এই সকল কথা লিখিয়ো না। তাহাতে আমার মনে অত্যন্ত যাতনা হইয়া থাকে। এ সংসারে ভাবনা আমার তোমার জন্য।
অকস্মাৎ তাঁহার আয়ত নয়নদ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হইল এবং আমরা সবিস্ময়ে দেখিলাম দরদরধারায় তাহা নিগলিত হইয়া দরদরধারে তাঁহার গণ্ডদ্বয় প্লাবিত করিয়া নামিয়া আসিল।
পিতৃদেব অত্যন্ত অভিভূত হইয়া গেলেন, বলিলেন—তুমি ক্রন্দন করিতেছ সতীবউ?
মাতা নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সে-মূর্তি অপরূপ। এমন কদাচ নিরীক্ষণ করিয়াছি। মুখমণ্ডল যেন ঈষৎ ঊর্ধ্বে তুলিয়া তিনি কোন্ অদৃশ্যলোকের দিকে তাকাইয়া আছেন। এবং সেখানে যাহা কিছু সংঘটিত হইতেছে, তাহা তিনি দিব্য দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিতেছেন।
আমি তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিয়া ডাকিলাম–মা।
তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন-রত্ন বাবা, তাঁহার ভাগ্যে আমার জন্যই দুঃখভোগ রহিয়াছে। তুমি আমাকে একটি প্রতিশ্রুতি দাও যে, আমার অবর্তমানে উনি যাহাই করুন, তুমি কদাচ তাহাকে অভক্তি করিবে না, অবহেলা করিবে না।
আমি কহিলাম—সে কি মা? এমন বাক্য তুমি কেন কহিতেছ? আমি কি নরাধম? আমি কি মনুষ্যবর্জিত?
মাতৃদেবী কহিলেন—না বৎস, তুমি অতি কঠোরচেতা ন্যায়বান বলিয়াই এরূপ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাহা ছাড়াও আরো একটি কথা রহিয়াছে। তোমরা ধনবান, তোমরা ভূসম্পত্তিশালী রাজতুল্য ব্যক্তি। তাহাদের মধ্যে এমতপ্রকারের মতিভ্রম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘটিয়া থাকে। পূর্বে রাজাদের বাদশাহদের মধ্যে এরূপ ঘটনা নিরন্তর ঘটিয়াছে। আজও ধনসম্পত্তি লইয়া পিতাপুত্রে মনোমালিন্যের অবধি নাই।
বলিয়া তিনি বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মার্জনা করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।
পিতা সকরুণ হাস্যসহকারে বলিলেন—উঁহার কথা তুমি ধর্তব্যের মধ্যে আনিয়ো না রত্নেশ্বর। দেবতা-দেবতা, ধর্ম-ধর্ম করিয়া তাঁহার মস্তিষ্ক সকল সময় সুস্থ থাকে না। বিশেষ করিয়া পূজা করিয়া উঠিবার অব্যবহিত পরই। অনেক সময় তিনি এইরূপ আবোল-তাবোল বকিয়া থাকেন। অতঃপর—।
তারপর রত্নেশ্বর তাঁর ডায়রীতে এদেশের তৎকালীন ধর্মবিশ্বাসের অজ্ঞতা সম্পর্কে অনেক কথা লিখেছেন। বলেছেন—এইসব ‘ভর’ দেবাবিষ্ট বা ভূতাবিষ্ট হওয়ার মতোই মানসিক বিকার। মা যে বারো বৎসর ব্রত করেছিলেন তাতে কি তাঁর বাপের পাপের খণ্ডন হয়েছে? হয়নি। এইসব অলীক বিশ্বাস আমাদের সর্বনাশ করেছে। আমি এসব থেকে দুরে থাকব।
যাক, এইবার যা ঘটল, তাই বলি। রত্নেশ্বর রায় ফিরে এলেন কীর্তিহাট। কলকাতা থেকে হুইস্কী-ব্রান্ডির কেস এল, টার্কী ফাউল, তার সঙ্গে ডজন দরুণে দেশী মুর্গী, ভাল দেখে ভেড়া, কলকাতার মিষ্টান্ন। বিভিন্ন সাহেব-অফিসারদের এবং তাঁদের স্ত্রীর জন্যে সোনার ঘড়ি, সিল্কের থান, গরম কাপড়ের থান, মূল্যবান লেডীজ শাল এল। বিশেষ ব্যবস্থা করে কলকাতা থেকে সাহেবদের প্রিয় ফুল, তা-ও আনানো হয়েছিল। তবে সেগুলো মেদিনীপুর শহর পর্যন্ত পৌঁছুতে তাজা থাকেনি।
রত্নেশ্বর রায় চোগা-চাপকান পেন্টালুন পরে মাথায় শামলা লাগিয়ে বুকের উপর কাটাকাটি চিহ্নের মত ধাঁচে কাশ্মিরী শাল ফেলে সাহেবদের বাংলোয় বাংলোয় বড়দিনের ভেট দিয়ে সাহেবদের অজস্র ধন্যবাদ দিয়ে কীর্তিহাট ফিরে এসেছিলেন।
ওদিকে শ্যামনগর কেনা গিয়েছিল। বীরেশ্বর রায় যা বলেছিলেন, তাই সত্য হয়েছিল। ট্যারা দে-সরকার নিজে এসেছিলেন হুগলী শহর। শ্যামনগর হুগলী জেলায়। সেখানে কীর্তিহাটের রায়দের এস্টেটের সেরেস্তা ছিল, নিজেদের বাড়ী কিনেছিলেন। একটা সে-আমলের পুরনো ওলন্দাজদের কুঠী। সেই বাড়ীতে ট্যারা দে-সরকার ভাঙা হাত নিয়ে পুত্রের হাত ধরে এসে রত্নেশ্বর রায়ের সামনে প্রথম হেঁট হয়ে নমস্কার করে বলেছিলেন—বৈষ্ণব হয়ে তুলসীপত্র একটিকে ছোট দেখে ঠিক ঠাওর করতে পারিনি বাবা, মনে হয়েছিল তুলসীপাতা নয়, পুদিনার পাতা। পায়ে মাড়িয়ে গেলাম, একটু ঠাওর করেও দেখলাম না। তা ডান হাতখানাই ভেঙে গেল!
আচার্য ছিলেন, তিনি বলেছিলেন—হবে। আবার ডান হাত হবে দে-সরকার। পায়ে মাড়ানো তুলসীপাতা মাথায় তুলে ধরলে যখন তখন আবার হবে। তবে ওই কিঞ্চিৎ বেঁকে থাকবে।
—হবে? আচার্যমশায় বলছেন—আবার হবে?
—হবে বৈকি! সত্যনারায়ণের পাঁচালী তো শুনেছ? সেই যে বণিকের মেয়ে সত্যনারায়ণের প্রসাদ খেয়ে নিতে যাবে এমন সময় খবর এল-নদীর ঘাটে বাপ- স্বামী সাতখানা বোঝাই নৌকা নিয়ে ফিরেছে, অমনি
—হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে থাকা কি, মুখস্ত আছে। ‘পাক দিয়া ফেলে রামা হস্তের প্রসাদ।’
—হ্যাঁ, অমনি নৌকোসমেত স্বামী ঘাটের মুখে বার কয়েক বোঁ বোঁ করে ঘুরে ভুস করে জলের তলায় চলে গেল। ঘাটের জলের উপর শুধু বুক-বুক করে বুক-বুকি উঠল। তার দৈববাণী—আমার প্রসাদ ফেলে কোন্ অহঙ্কার?’ যা—এখন মাটি শুধু চেঁচে তুলে খা। তাহলে স্বামী নৌকো উঠবে। তা সে মেয়েটা খেয়েছিল, আর স্বামী সমেত নৌকো যেমন ভুস করে ডুবেছিল, তেমনি আবার হুশ করে উঠেছিল। হবে আবার তেমনি হবে।
রত্নেশ্বর এঁদের এই বিচিত্র কথোপকথন কৌতুকের সঙ্গে উপভোগ করেছিলেন। কথাগুলো তিনি ডায়রীতে লিখে রেখেছেন।
আচার্য দে-সরকারদের কাছে হাজারদুয়েক টাকা গোপন দালালি পেয়েছিলেন, সে খবর রত্নেশ্বর রায়ের কাছে গোপন ছিল না। তিনি মুখে কিছু বলেননি। দে-সরকার যখন তাঁর সম্পত্তি লাখেরাজ করে দেবার প্রস্তাব জানিয়েছিলেন, আচার্য তা সমর্থন করেছিলেন প্রকারান্তরে। কিন্তু সে নামে। তিনি রত্নেশ্বরকে চিনেছিলেন। রত্নেশ্বর রায় বীরেশ্বর রায়ের উপদেশ মনে করে সম্পত্তি মোকররী-মৌরসী করে দিয়েছিলেন—বিঘায় দু’আনা খাজনা মোট খাজনা, ধার্য হয়েছিল বত্রিশ টাকা কয়েক আনা। আচার্য বলেছিলেন—ওঁদের ভিটে দেবতার ঘর-এগুলি সম্বন্ধে আমি বলি—লাখরাজ করে দেওয়া হোক।
দলিল হয়েছিল বিমলাকান্তের নামে। এবং সঙ্গে সঙ্গেই আর দুটো দলিল হয়েছিল—পাট্টা আর কবুলতি। জমিদার বিমলাকান্ত শ্যামনগর-রাধানগর পত্তনী বিলি করেছিলেন কীর্তিহাটের মা আনন্দময়ীর সেবায়েত বীরেশ্বর রায় এবং রত্নেশ্বর রায়কে।
শ্যামনগরের ব্রাহ্মণ-বৈদ্য, সােপ-মাহিষ্য বাসিন্দারা চব্বিশপ্রহর হরিনাম উৎসব করেছিল- বোল হরি বোল, বোল হরি বোল, বোল হরি বোল! দে সরকারদের বাড়িতে বিগ্রহের সামনে হরিবোল দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় ধ্বনি দিয়ে গিয়েছিল—বল হরি—হরি বোল!
একমাস পরে আবার কলকাতা থেকে পত্র এসেছিল।
“তুমি অবিলম্বে বধূমাতাকে লইয়া এখানে আসিবে। মাঘ মাস শেষ হইতে চলিল। আশা করি ইতিমধ্যে আদায়পত্রের কার্যাদি সুচারুরূপে নির্বাহ হইয়াছে। আমরা ফাল্গুনের প্রথমেই পশ্চিম যাত্রা করিতেছি। তোমাকে যে সকল দলিলের কথা বলিয়াছিলাম, তাহা অ্যাটর্নী প্রস্তুত করিয়াছেন। তুমি আসিলেই রেজিস্ট্রি হইবে। মাসিমাতাকে বলিবে—তিনি যদি তীর্থে যাইতে চান, তবে আসিতে পারেন। অঞ্জনার কথা উঠিয়াছিল। কিন্তু মাসিমাতা থাকিবেন না, সুতরাং তাহার যাওয়া হইবে না। মাসিমাতাকে বলিবে- সোফিয়া বাঈ আমাদের সঙ্গে আজমীঢ় যাইবে, তিনি যেন তাহা বিবেচনা করিয়া দেখেন।”
প্রায় ছ’ মাস পরে বীরেশ্বর রায় কলকাতা ফিরেছিলেন। তিনি তখন একা। ভবানী দেবী নেই। তিনি যা বলেছিলেন, তাই হয়েছিল। বীরেশ্বর রায় আবার তখন মদ্যপান শুরু করেছেন। সুরেশ্বর বললে—কীর্তিহাটের কড়চায়, রায়বাড়ীর জবানবন্দীতে, বীরেশ্বর রায়ের শেষজীবন-বছর তিনেক বলতে পার-হারিয়ে যাওয়া মানুষ।
তাঁর কথাটা সেরে নিই সুলতা। ভবানী দেবীর মৃত্যু আমি এঁকেছি। কিন্তু বীরেশ্বর রায়কে তারপর আর আঁকি নি। তিনি—
যাক, বীরেশ্বর রায় এবং ভবানী দেবীর জীবনের কথাটা গুছিয়েই বলি। রায়বাড়ীর জবানবন্দীর এই ছবিগুলির দিক থেকে দৃষ্টি একটু সরিয়ে নাও।
বীরেশ্বর রায় ভ্রমণকাহিনীর কথা লেখেন নি। কিছু পাই নি, তবে লোকজন যারা সঙ্গে গিয়েছিল, তাদের বলা কথা রায়বাড়ীতে কিছু কিছু আজও বেঁচে আছে। এবং একটা জমা-খরচের ছোট খাতা আছে।
যারা সঙ্গে গিয়েছিল, তারা সবাই চাকর-বাকর, দারোয়ান, ঠাকুর। এই সব একটু বিস্ময়কর ঠেকবে সুলতা যে, এদের মধ্যে গোপাল সিংও ছিল। বড়হুজুর তীর্থে যাবেন শুনে রত্নেশ্বরের অনুমতি নিয়ে সে কলকাতায় এসে বড় হুজুরের কাছে হাত জোড় করে বলেছিল—হুজুরের কিরপা হলে সে মহাপাপ থেকে মুক্ত হতে পারে। তাকে হুজুরবাহাদুর এত লোকজনের সঙ্গে তাঁবেদার হিসেবে গরিবকে ভি সঙ্গে নিয়ে চলেন। সে গয়াতে গিয়ে বেটাকে পিণ্ড দেবে, বাপ দাদাকে দেবে। কাশী আর প্রয়াগমে গিয়ে স্নান-অর্চনা করে সে সব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে!
বীরেশ্বরের আগেই ভবানী দেবী বলেছিলেন—তুমি যাবে গোপাল সিং, তুমি যাবে।
বীরেশ্বরের মাসিমা রত্নেশ্বরের ঠাকুমাও গিয়েছিলেন। আর বলেছি, সোফিয়া বাঈও সঙ্গে গিয়েছিল। তার ব্যবস্থা সব আলাদা ছিল, কিন্তু খাওয়া-শোয়ার সময় ছাড়া অন্য সময়ের বেশীর ভাগটা থাকত বীরেশ্বর রায়ের কাছে। বাঈজীর ঢঙ বা বেশভূষায় মুসলমানী ভাব তার ছিল না। সেই দীর্ঘকাল পর প্রথম সে যে লালপেড়ে শাড়ী হিন্দুস্থানী ঢঙে পরে এসেছিল, তাই ছিল তার পোশাক। সন্ধ্যার পর সে যখন এসে গানের আসর পাতত, তখনই কিছুটা প্ৰসাধন এবং সামান্য বেশভূষা করে আসত।
রেললাইন তখন হাওড়া থেকে উত্তরমুখে উত্তরাপথে চলেছে দ্রুতবেগে। কাজ মিউটিনির কয়েকবছর আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। ১৮৫৫ সালে লুপ লাইনের কাজ চলছিল, তিনপাহাড়ি, সাহেবগঞ্জ অঞ্চলে, এদিকে মেন লাইন গিয়ে পৌঁছেছিল রাণীগঞ্জ। ১৮৫৫ সালে রেললাইনের তিন জন সাহেব সাঁওতালদের মেয়ে কেড়ে নিয়ে খুন হয়েছিল ইতিহাসে আছে। সে সময় কীর্তিহাটের জেলা মেদিনীপুরেও সাঁওতালেরা ক্ষেপেছিল। মিউটিনির পর রেললাইন দ্রুততর বেগে তৈরী হয়ে এগিয়ে চলেছিল। স্টীম ইন্জিনে টানা ট্রেনের বগিতে চড়ে পনের দিনের পথ তিনদিনে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু বীরেশ্বর রায় ট্রেনে চড়েন নি। তিনি গিয়েছিলেন বজরায়
চিকিৎসকের উপদেশের জন্যও বটে এবং তাঁর মেজাজের জন্যও বটে। রেলগাড়ী—সে ছুটবে আপন গতিতে, আপন নিয়মে এবং আরাম তাতে সীমাবদ্ধ। তাছাড়া খাওয়া-দাওয়া নিয়ে ভবানী এবং তাঁর সঙ্গে মাসিমা প্রভৃতি ক’জন বিধবার রেলগাড়ীতে দারুণ অসুবিধা। সে আমল—রেলগাড়ির বিভিন্ন কামরায় কত জাতের কত লোক, গাড়িগুলো পৃথক হলেও একসঙ্গে জোড়া; এর মধ্যে কি জাত বাঁচিয়ে খাওয়া যায়?
বীরেশ্বর রায়ের অসুবিধা, রেলগাড়ী তাঁর হুকুম মানবে না। তাঁর জীবনের কার্যসূচীগুলোর সব ওলোট-পালোট হয়ে যাবে। তার উপর ট্রেনে ঝুঁকি আছে। আর আছে উল্টে পড়া কি সামনাসামনি দুটো ট্রেনে ধাক্কা লাগবার ভয়। চিকিৎসকেরাও বলেছেন, এই ধাক্কা ধকলে বীরেশ্বর রায়ের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে পারে। তার থেকে, তাঁরাই বলেছেন—বজরায় যাওয়াই উচিত। ধাক্কা-ধকল থাকবে না, এখন ফাল্গুন মাস, ঝড় বা হাওয়ার সময় নয়। বজরা নৌকো যাবে মসৃণ গতিতে। মানসিক স্বস্তিতে থাকবেন রায়। এ ছাড়াও এই গঙ্গার বাতাসের গুণে রায়ের স্বাস্থ্য আরো ভাল হয়ে উঠবে বলেই তাঁদের বিশ্বাস। তাই হয়েছিল।
তিনখানা বজরা, দুখানা বড়, একখানা ছোট। সব থেকে বড় বজরাখানা বীরেশ্বর রায়ের আমলের নতুন বজরা, যাতে দুখানা কামরা। একখানা বসবার, একখানা শোবার। এই বজরাতেই কীর্তিহাট যাওয়া-আসা করতেন। আর একখানা বজরা ছিল, সোমেশ্বর রায়ের আমলের, ছোট বজরা, সেটায় ছিল সোফিয়া বাঈ। অন্য বড় বজরাখানায় ছিল ভবানীদেবীর পূজার ব্যবস্থা, রান্নার ব্যবস্থা, এইটেরই একটা কামরায় থাকতেন মাসিমা এবং আরো দুটি বিধবা আত্মীয়া।
আর বাদবাকি লোকজন সব ছিল কয়েকখানা নৌকোয়। ভবানী দেবীর নিয়ম ছিল, ভোরবেলা উঠে ঘাটে নেমে স্নান করে পুজোর নৌকায় উঠতেন। এদিকে লোকজনেরা মুখ-হাত ধুয়ে মুড়ি-মুড়কি-চিঁড়ে-গুড়, কাছের বাজার থেকে দই কিনে ভিজিয়ে এক পেট খেয়ে নিত। মাল্লা-মাঝিদের অনেকে ভোররাত্রে উঠে ভাতে-ভাত ফুটিয়ে খেয়ে তৈরী হত। ওদিকে মাসিমারা ও স্নান সারতেন। তখন নৌকো ছাড়ত।
সোফিয়া বাঈয়ের কথা বলতে ভুলছি। সেও উঠত খুব ভোরে। উঠে স্নান করে বজরায় গিয়ে ঢুকত। কাপড়-চোপড় ছেড়ে ছাড়াতে বসত মেওয়া ফল। বাদাম, পেস্তা, কিসমিস ভেজানো থাকত রাত্রে। তার সঙ্গে কাটত ফল। বাজার থেকে টাটকা ভাল যা পাওয়া যেত তাই।
রায় উঠতেন একটু বেলায়। নৌকা চলতে থাকত, তখনই তিনি উঠতেন। কোনোদিন দেড় ঘণ্টা, কোনোদিন দুঘণ্টা পর উঠতেন তিনি। তখন আবার একবার বজরা থামত। তিনি একবার তীরে নামতেন। কিছুখানি হাঁটতেন। শরীরটাকে একটু চঞ্চল করে নিয়ে প্রাতঃকৃত্য সেরে আবার নৌকায় উঠতেন। মুখ হাত ধুয়ে কাপড়-চোপড় বদলে বসতেন বসবার ঘরে। এদিকে সোফিয়ার বজরা থেকে রূপোর রেকাবিতে কাটা ফল, মেওয়া ফল এসে পৌঁছুত, ভবানী দেবীর বজরা থেকে আসত মিষ্টান্ন এবং দুধ। তারপর চাকর বানাত চা। নটা, কোনোদিন দশটাও বাজত খাওয়া শেষ হলেই বজরাখানা মাঝগঙ্গায় থামত। ওদিকে পাশে এসে লাগত সোফিয়া বাঈয়ের বজরা। মাঝখানে দুপাশে রেলিং দেওয়া তক্তা পেতে দিত মাঝিরা। বাঈ তাঁর বীণাখানি হাতে করে এসে উঠতেন হুজুরের বজরায়।
এসে সেলাম করে বসত; তার জন্যে পাতা থাকত স্বতন্ত্র গালচে, সঙ্গে কেউ না, সারেঙ্গীদার বা তবলচী কেউ না। বসে বীণা বাজাতো। কখনো উৎসাহবোধ করলে নিজেই বীরেশ্বর রায় তবলচী সারেঙ্গীদের ডাকতেন। সে ক্বচিৎ। কারণ এর ঘণ্টাখানেক পরই বজরা আবার একবার দাঁড়াত। এবার সোফিয়া চলে যেত নিজের বজরায়। তারপর তার বজরা সরে গেলে এপাশে এসে লাগত ভবানী দেবীর বজরা। ভবানী দেবীর বজরা এবং সোফিয়ার বজরা একসঙ্গে ঠেকলে বীরেশ্বর রায়ের মাসিমা আপত্তি করতেন।
—ঠাকুর-দেবতা, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থার সঙ্গে স্পর্শ-দোষ ঘটবে।
যাক। আবার বিকেল হতে হতে আসত সোফিয়া। এবার সাজসজ্জা কিছু করতে হত তাকে, সারেঙ্গীদার, তবলচি, সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে আসর পড়ত। ভবানী দেবীও বজরায় থাকতেন। কিছু রাত্রি হলে তবে ভবানী দেবী আসতেন। স্বামীর খাবার-দাবার নিয়ে। সন্ধের মুখে বজরা নৌকো কোন একটা বাজার বা গঞ্জের ঘাটের আশে-পাশে বাঁধা হত। রাত্রিকালে চলার নিয়ম ছিল না। আর একবার দুপুরে নৌকো বাঁধা হত, লোকজনেরা রান্না করে খাবে।
প্রথম এসে নৌকো বজরার বহর তাঁরা বেঁধেছিলেন পাটনায়। ওখান থেকে পথে পথে যাবেন গয়া। পালকি, বয়েল গাড়ী নিয়ে গয়া যাবেন। সেখান থেকে ফিরে পাটনার ঘাট থেকে আবার রওনা হবেন কাশী। গোটা বৈশাখটা থাকবেন কাশীতে, তারপর রওনা হবেন প্রয়াগ। প্রয়াগ থেকে যমুনায় ঢুকে মথুরা-বৃন্দাবন; আগ্রা-ফতেপুরসিক্রি; আকবর শাহের সমাধি। তারপর এখনো ঠিক হয় নি, দিল্লী যাবেন কি গোয়ালিয়র যাবেন। গোয়ালিয়রের মিঞা তানসেনের সমাধি আছে। দিল্লী থেকে হরিদ্বার যাবার ইচ্ছা, ওদিকে কুরুক্ষেত্র, সাবিত্রীতীর্থ জয়পুর এবং আজমীঢ়। আজমীঢ়ে সোফিয়া বাঈ বিদায় নেবে বলেছে।
বীরেশ্বর রায় সঙ্গে অর্থ নিয়েছিলেন যথেষ্ট। কত নিয়েছিলেন তার জমা-খরচ নেই। গয়াতীর্থে পিতৃপুরুষকে পিণ্ড তিনিও দিয়েছিলেন, ভবানী দেবীও দিয়েছিলেন। এই প্রথম শ্যামাকান্তকে তাঁর গৃহী নামে পিণ্ড দিয়েছিলেন। স্বামীকেও অনুরোধ করেছিলেন—সমাজের ভয়ে সেখানে তাঁর শেষ কাজ করতে পারিনি। এখানে করলাম। তুমিও তোমার কাজ কর। আমার বাবাকে এখানে তুমি পিণ্ড দাও। সেও দিয়েছিলেন বীরেশ্বর রায়।
***
সুলতা, যেটুকু শুনতে পাই; তাতে শুনি এই গয়া থেকেই ভবানী দেবী কেমন পাল্টে গিয়েছিলেন। পিণ্ড দিয়ে এসে স্বামীকে বলেছিলেন—আমার কাজ শেষ হল গো! এইবার তুমি খালাস দিলেই আমি খালাস!
বীরেশ্বর বলেছিলেন-সে আমি যাবার সময় দিয়ে যাব, তার আগে নয়। অপেক্ষা করে থাক।
ভবানী বলেছিলেন—ওকথা বলতে নেই, বলো না।
—তুমিও খালাস চেয়ো না!
কথাটা ওখানেই শেষ হল, কথার মধ্যে। কিন্তু সঙ্গের লোকেরা এখানে ফিরে এসে বলেছিল—কথা শেষ হলে কি হবে; কাজে, ওই দিন থেকেই শুরু হল।
ভবানী দেবী কেমন যেন বদলে যেতে লাগলেন; আচ্ছন্ন হয়ে থাকতেন একটা কোন ধ্যানে। ধ্যান কথাটা তাদের সুলতা; একাল হলে অন্য কথা বলত নিশ্চয়। কোন একটা চিন্তায়, কিংবা নিজের জীবনের সংস্কারের আচ্ছন্নতায়।
গয়া থেকে পাটনা ফিরবার পথে এটা ঠিক ধরা যায় নি। কারণ পাল্কীতে এসেছেন। পথে চটিতে আশ্রয় নিয়েছেন রাত্রে। বীরেশ্বর রায়ের কাছে এটা ধরা পড়ল পাটনায় ফিরে, বজরায় কাশীর পথে। প্রথম দিনই ভোরে গঙ্গাস্নান করে তাঁর পুজোর ঘর যে বজরায়, সেই বজরায় উঠে পুজোয় বসলেন। সকাল বেলা সেদিন বীরেশ্বর রায় একলা পড়ে গেলেন। সোফিয়া বাঈ পাটনা সিটিতে গিয়েছিল, এক বান্ধবী বাঈজীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য। বীরেশ্বর রায়ের অনুমতি নিয়েই সে গিয়েছিল। বীরেশ্বর রায় একখানা ইংরিজী বই পড়ছিলেন। ভেবেছিলেন বই পড়েই সময়টা কেটে যাবে। কিন্তু সময় দীর্ঘ হলে তিনি কি করবেন? বেলা প্রায় এগারটা অতিক্রান্ত হতে চলল, তবু ভবানী এলেন না তাঁর পূজার নির্মাল্য নিয়ে। সোফিয়া নির্দিষ্ট সময় ফিরে সরাসরি উঠল তার বজরায়। কারণ এই সময়টা সে থাকত না। ভবানী দেবী জল খান, এই কর্তব্যটির পর। এ সময় সোফিয়া থাকলে তাঁর মন খুঁত-খুঁত করত।
জানবাজারের বাড়ীতে সোফিয়া বসে থাকত মেঝের উপর পাতা গালিচায়, বীরেশ্বর রায় বসে থাকতেন একটা বড় ডিভানে ঠেস দিয়ে। অথবা দামী সেগুন কাঠের পালিশ-করা খাট জাতীয় তক্তপোশের উপর বড় তাকিয়া ঠেস দিয়ে। সেখানে দোতলার মেঝে হলেও সেটা পড়ত মা ধরিত্রীর অংশের পর্যায়ে। সেখানে ছোঁয়া গণ্য হত না। কিন্তু বজরার কাঠের মেঝে তা নয়। একটু এগিয়ে এসে সুরেশ্বর বললে—বৃহৎ কাষ্ঠে দোষ নেই, একথাটা ভবানী দেবী বা তাঁর মাসিশাশুড়িরা মানতেন না।
সেই কারণে সোফিয়া ফিরে এসে এ বজরায় ওঠে নি। সে নিজের বজরায় গিয়ে উঠেছিল।
তার রান্নাবান্না আছে। খাওয়া-দাওয়া আছে। তারও নিজের কিছু ভজন আছে। তার ভজনও নানান যোগের জটিলতায় জটিল। ইসলামী উপাসনার সঙ্গে তার আর একটা জপ ছিল, সেটা পাগলাবাবার দেয়া মন্ত্র জপ।
বীরেশ্বর রায় অধীর হয়ে মহিন্দরকে বলেছিলেন—কি হল দেখ তো মহিন্দর? এখনো পুজো শেষ হল না? এত দেরী তো হয় না!
প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভবানী দেবী এসে উঠেছিলেন তাঁর বজরায়।
বীরেশ্বর রায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন—এত দেরী আজ?
একটু বিস্মিত হয়েই ভবানী বলেছিলেন—দেরী? না তো!
—না তো? দেখ তো ঘড়িতে কটা বাজল?
ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ভবানী বলেছিলেন—তাই তো! এগারোটা! আমি তো বুঝতে পারি নি!
সেদিন আর এ নিয়ে উচ্চবাচ্য হয় নি। ভবানী দেবী চরণোদক নির্মাল্য দিয়ে কাপড় ছেড়ে এসে স্বামীর পাশে বসেছিলেন।
বীরেশ্বর তখনও প্রায় যুবক, জন্ম তাঁর বিশ সালে। তখন চলছে আঠারশো ষাট। চল্লিশ বছর বয়স। তবুও জীবনে যে যুদ্ধ তিনি করেছেন নিজের সঙ্গে, যে যুদ্ধের নিষ্ঠুর আঘাতে তাঁর বাঁ হাত, বাঁ পা খানিকটা দুর্বল হয়ে গেছে, তারই ফলে তখন তাঁর চুলের মধ্যে দু-চারটে পাকা চুল দেখা যেতো; ভবানী পাশে বসে তাই খুঁজে খুঁজে বের করে তুলে ফেলতেন।
সেদিন তিনি বলেছিলেন—আজ সকাল থেকে গান শোনা হয় নি, না?
—হ্যাঁ, সোফিয়া তার এক সহেলীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল।
—এখনো ফেরে নি?
—সে ঠিক সময় ফিরেছে। সে বলেছিল—দশ, সাড়ে দশ বাজে লৌটঙ্গী, ঠিক তাই এসেছে। কিন্তু তোমার আসবার সময় হয়েছে বলে বজরায় ওঠে নি।
—ও, তাই আমার রাজাবাহাদুরের মেজাজ খারাপ হয়েছে!
—তোমার তাই ধারণা, না?
—তাতে অন্যায়টা কি হল?
ভবানী দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে উঠেছিল বীরেশ্বরের। বলেছিলেন—তুমি বুঝতে পার না ভবানী, আমি তোমাকে কেমনভাবে পেতে চাই? কিন্তু তুমি নিজেকে এমন আড়াল করে রেখেছ, পুজো পুজো আর পুজো নিয়ে—!
ভবানী দেবী সেদিন অপ্রস্তুত হয়ে বলেছিলেন—দেখ তো পাগলামি! হ্যাঁ গা, আমি পুজো-অর্চনা করি কি আমার মঙ্গলের জন্যে?
বীরেশ্বর বলেছিলেন—থাক!
ভবানী ডেকেছিলেন মহিন্দরকে মহেন্দ্র, বাবুকে তামাক দাও নি কেন? তামাক দাও না। এক কাজ কর তো! বজরা থেকে আমার তানপুরাটা নিয়ে এস তো! পাখোয়াজটাও আনো। ময়দা করো।
স্বামীকে বলেছিলেন—নাও, আজ অধীনী তোমাকে গান শোনাবে। মহিন্দর তানপুরা এনে দিতেই বলেছিলেন-বজরা খুলে মাঝগঙ্গায় নিয়ে যেতে বল। ঘাটের কাছে ভিড় জমে যাবে। আর ও বজরায় মাসিমারা আছেন। সোফি বাঈকেও ডাক।
—না। বীরেশ্বর মানা করেছিলেন। তুই তানপুরা পাখোয়াজ দে। সোফি থাক।
ঘাট থেকে বজরা খুলে মাঝগঙ্গার দিকে চলতে আরম্ভ করেছিল। সকলে বিস্মিত হয়েছিল, কিন্তু মহিন্দর চাকর বজরার ছাদে উঠে বলেছিল, একটু ঘুরে আসতে চলল বজরা।
***
এ বিবরণ মহিন্দরের। সে তীর্থযাত্রা থেকে ফিরে এসে রত্নেশ্বর রায়কে বলেছিল। রত্নেশ্বর তাঁর ডায়রীতে লিখে রেখেছেন।
সেদিন নাকি বড়হুজুরের যে আনন্দ, হুজুরের তেমন আনন্দ মহিন্দর আর কখনো দেখেনি। গান গাইতে গাইতে তানপুরার হাত মায়ের বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দুচোখ থেকে ধারা নেমেছিল।
গান সে আশ্চর্য গান, আর হুজুরের সে বাজনাও আশ্চর্য! গান থামল, পাখোয়াজে ঘা মেরে হুজুর চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—আমি ভাল হয়ে গিয়েছি। সতীবউ, আমি ভাল হয়ে গিয়েছি। ভবানী দেবী প্রথমটা বুঝতে পারেন নি। তিনি তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলেন সবিস্ময়ে। বীরেশ্বর রায় বলেছিলেন—বাঁ হাতে আমার একটু কষ্ট হল না! আমি ভাল হয়ে গিয়েছি!
বিকেলে গঙ্গার কিনারায় উঠে দারোয়ানের সঙ্গে ঘুরেও এসেছিলেন। লাঠির দরকার হয় নি, তবু হাতে ছড়ি না নিলে যেন কেমন হাতখানা স্বস্তি পাচ্ছিল না।
***
পরের দিন ভোরে নৌকা বজরা পাটনা ছেড়ে রওনা হয়েছিল কাশীর মুখে। সে দিনও দুপুরে গান গেয়েছিলেন সতীবউরাণী। সেদিন কিন্তু পাখোয়াজ ধরতে দেন নি স্বামীকে। বলেছিলেন—বাঁয়া তবলা নাও। কাল যা পাখোয়াজে ঝড় তুলেছ, ও চলবে না। ভাল হয়েছ, বেশ ভাল কথা। কিন্তু ও হাত নিয়ে যুদ্ধ করা চলবে না।
সেদিন ভবানী দেবী ধ্রুপদী গান নি। হাল্কা গান ধরেছিলেন। সেদিন গানের আসর ভাঙতে আরো বেলা হয়েছিল। খেতে অনেক দেরী হয়ে গেল। ভবানী দেবী বললেন-না, এ হবে না। কাল থেকে রাত্রে, সোফির আসরের পর আমি গান শোনাব। না হয় এ বেলা সোফি বেশীক্ষণ গান শোনাবে, রাত্রে ওর আসর সকাল সকাল ভেঙে দিয়ো, তারপর আমাদের পালা।
তাই চলেছিল ক’দিন। বড় আনন্দ চাকর-বাকরদের। গান-বাজনা নিয়ে হুজুরের ঝোঁক বাড়ল। নতুন নিয়ম হ’ল, বেলা থাকতে নৌকো বাঁধতে হবে। হুজুর কিনারায় উঠে খানিকটা করে হাঁটবেন।
স্নানের আগে তেল মেখে হুজুর নিজে হাত-পা ভেঁজে নিতেন। ডন-বৈঠক দেবার মতলবও করেছিলেন, কিন্তু তাতে সতীরাণী-মা বাধা দিয়ে বলেছিলেন—না। যা রয়-সয়, তাই কর। করতে আমি দেব না।
দিন দশেক পর, কাশী পৌঁছুবার দুদিন আগে, হুজুর সেদিন যেন একটু বেশী মেতে উঠলেন। মদ খেয়ে নয়, নিজের ঝোঁকে। সেদিন বললেন—অনেক দিন নাচ হয় নি, আজ নাচ হবে।
সতীরানী-মা বারণ করলেন—না।
হুজুর বললেন–না কেন? অনেক দিন নাচের আসর বসে নি, আজ এক বছরের ওপর। সোফি বাঈ মাফি চাইলে। হাত জোড় করে। তবু শুনলেন না। নাচ হল শেষ পর্যন্ত। সে এক প্রহর রাত পর্যন্ত।
সেও আসর জোর করে ভেঙে দিলেন বউরানী। সোফি বাঈ চলে গেল। এই পর্যন্ত মহিন্দর জানে।
এর পর রাত্রে কি হল স্বামীস্ত্রীর মধ্যে, কেউ জানে না। কিন্তু ভোরবেলা উঠে বউরানী গঙ্গাস্নান করে সেই যে পুজোর ঘরে ঢুকলেন, সারা দিনেও আর বের হলেন না। মাসিমা এসে চরণোদক পুষ্প দিয়ে বলে গেলেন, আজ আর বউমা পুজোরঘর থেকে বেরুবে না বাবা। কাল কাশী পৌঁছুবে, সে আজ সংকল্প করেছে হবিষ্যান্ন করবে। কম্বলে শোবে। শোবেও ওই পুজোর ঘরে। বললে—ওঁকে কাল বলা হয়নি। ভুলে গেছি বলতে। ওঁকে আপনি বলে দেবেন। আজ আমি ও বজরায় যাব না। সোফিকে একটু বেশিক্ষণ থাকতে বলেছে। এবেলা ওবেলা দুবেলাই।
বীরেশ্বর রায় একটি কথাও বলেন নি। চুপ করে শুনে শুধু একটি হুঁ বলেছিলেন। তারপর চুপ হয়ে গেলেন।
সেদিন স্নানের সময় তেল মেখে ডন-বৈঠক দিলেন। বিকেলবেলা অন্যদিনের চেয়ে বেশীক্ষণ বেড়িয়ে ফিরলেন।
সন্ধেবেলা সোফি বাঈয়ের গানের আসর বসে ভাঙল প্রথম প্রহরের বদলে রাত দু প্রহরে। গঙ্গার পাড়ে চারিদিকে তখন কোলাহল করে শেয়াল ডাকছে।
পরের দিন বেলা দশটার সময় নৌকো কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর লাগল। ও বজরার বাইরে এসে দাঁড়িয়ে বেণীমাধবের ধ্বজাকে এক পায়ে দাঁড়িয়ে মা প্রণাম করছিলেন। তাঁর সে চেহারা দেখে সকলে অবাক হয়ে গিয়েছিল।
এ তো পরশুর রাণীমা নন।
এ যেন সেই হুজুরের অসুখের সময় যে রাণীমা এসে শুধু শাঁখাশাড়ী পরে যোগিনীর মত রায়বাড়ীতে ঢুকেছিলেন, সেই রাণীমা!
একদিনের উপবাসও নয়, হবিষ্যান্ন করেছিলেন ভবানী দেবী, অর্ধ-উপবাসও বলা যায় না, সন্ধ্যার পূর্বে দুধ খেয়েছিলেন, তবু মনে হচ্ছিল, তিনি যেন কয়েকটা উপবাস করে আছেন; তার উপর চুল রুক্ষ; সংকল্পের জন্য উপবাসের পূর্বদিন তেল নিষিদ্ধ। কম্বলে শুতে হয়। অশৌচ পালনের মতই ব্যবস্থা। অলঙ্কার সব খুলে রেখে শুধু শাঁখা পরেই তিনি নেমেছিলেন। বিমলাকান্ত এসেছিলেন সস্ত্রীক, পাণ্ডার লোকজন উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব থেকে ব্যবস্থা করা ছিল। একটা বড় বাগিচাওয়ালা মোকাম ভাড়া করে রাখা হয়েছিল। পাল্কী-ডুলি এবং এক্কা হাজির ছিল। শহর থেকে একটু বাইরে। ভবানী দেবীর পরামর্শ মতই করা হয়েছিল সব। আর একটা বাড়িও ভাড়া করে রাখা হয়েছিল শহরের মধ্যে বিমলাকান্তের বাড়ির কাছে। কাশীতে এক মাসেরও উপর থাকবেন, বিশ্রাম নেবেন বীরেশ্বর রায়। গঙ্গার একেবারে ধারে। হরিশ্চন্দ্রের ঘাটের দিকে। বীরেশ্বর রায় ওই বাগানে থাকবেন, সঙ্গের দারোয়ান লোকজন সবই থাকবে সেখানে; শহরের বাড়ীতে থাকবেন মাসিমারা। ভবানী দেবী ভোরবেলা শহরের বাইরে বাড়ী থেকে পাল্কীতে চলে আসবেন শহরের বাড়ীতে। এখানে এসে সারাদিন থাকবেন, স্নান, পূজা-অৰ্চনা ইত্যাদি করবেন। বিকালবেলা বীরেশ্বর রায় আসবেন, সন্ধ্যায় দেবদর্শন সেরে বিমলাকান্তের সঙ্গে গল্পগুজব করে সস্ত্রীক ফিরবেন বাগিচাবাড়িতে। সোফিয়ার থাকবার ব্যবস্থা ওই বাগিচাবাড়ীতেই একটা আলাদা ছোট বাড়ীতে করা ছিল। সেটা ছিল বাগিচাবাড়ীর দপ্তরখানা বা বাইরের বাড়ী। মূল বড় বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ থাকলেও স্বতন্ত্র বাড়ি।
সুরেশ্বর বললে—এ-বাড়ী পরে কেনা হয়েছিল। এবং বাড়ীখানা পেয়েছিলেন মেজতরফ। মেজঠাকুরদা শিবেশ্বর রায়। শিবেশ্বর রায়ের ধর্মবিশ্বাস ছিল বলে রত্নেশ্বর রায় বাড়ীখানা তাঁকেই দিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছ থেকে এ-বাড়ী কিনেছিলেন আমার জ্যেঠামশাই—যজ্ঞেশ্বর রায়। এ-বাড়ী একবার আমি দেখেছি। আমার যখন পাঁচ-ছ বছর বয়স, তখন বাবা আমাকে এবং মাকে নিয়ে গোটা পশ্চিম ঘুরে এসেছিলেন, বড় মনোরম জায়গা ছিল। বাড়ীখানাও তেমনি মুঘল আমলের আমীরি ছাপমারা। কিন্তু সে-কথা থাক। যা বলছিলাম তাই বলি। এই বাইরের বাড়ী বা দপ্তর সেরেস্তাখানায় একখানা প্রশস্ত হল ছিল-সেইখানে বসত রাত্রের আসর।
মহিন্দর চাকর রত্নেশ্বর রায়কে বলেছিল—এই কাশী এসেই সব যেন গোলমাল হয়ে গেল। সতীরাণীমা ব্রত করলেন; ভোরবেলা যখন পাল্কীতে উঠতেন তখন আবছা অন্ধকারের মত দেখতাম, মায়ের যেন কেমন ঘোর লেগেছে। আবার ফিরতেন রাত্রে, তখন তাঁর দিকে তাকানো যেতো না। সে তখন কেমন মানুষ। “পিথিমীর নন।” খাওয়া-দাওয়া তো ফল-জল; তা ওই বাড়ীতে খেয়ে আসতেন। পাল্পী থেকে নামতেন যেন কাঁপছেন; দু’জন ঝি তাঁকে দু’পাশে ধরে উপরে নিয়ে যেত। এক মাস ব্রত, পয়লা বোশেখ থেকে বোশেখের সংক্রান্তি পর্যন্ত—তার মধ্যে প্রথম পনের দিন উপরে উঠেছিলেন, বাকী কদিন উপরে ওঠেন নি, তিনি আলাদা ঘরে শুতেন, তাঁর বিছানা একখানা কম্বল, তার উপর খুব ভাল রেশমী চাদর পাট করে চাদরের মত পাতা হত; আর একখানা কম্বল গুটিয়ে রেশমী চাদর জড়িয়ে বালিশের কাজ করত। আর চারখানা লালপাড় গরদের শাড়ী। শ্বেতপাথরের দু-তিনটে গেলাস, খান-দুই রেকাবি; আর জপের মালাটালা এইসব। বাক্সপেটরা যা সব আসল সামগ্রী, সে-সব থাকত রায় হুজুরের কামরায়। একেবারে জানালা খুললেই গঙ্গা।
মহাবীর সিং কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে ঘরের দরজায় পাহারা থাকত।
মহেন্দ্র রত্নেশ্বর রায়কে বলেছিল—মা ব্রত করতে লাগলেন, হুজুর যেন নতুন করে সেরে উঠলেন, মুখের উপর দাগ পড়েছিল, সেগুলো উঠে গেল, মনে হল দশ বছর বয়স কমে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আগের সেই মেজাজ। সেই চোখের তাকানি। সেই কড়া গলার ডাক। সব ফিরে এল।
রাত্রে সোফি বাঈয়ের আসর বসত অল্পক্ষণের জন্য। ওই মায়ের সঙ্গে ফিরে এসে; মাকে উপরে তুলে শুইয়ে দিয়ে সটান এসে উঠতেন বাইরের বাড়ীতে পাতা আসরে, একখানা গান শুনেই ফিরে এসে শুতেন। সোফি বাঈয়ের সঙ্গে আসর যা হবার তা হত দিনের বেলা। সকালে হুজুর উঠতেন আটটার সময়, তখন মা চলে গেছেন কাশীর ভিতরে শহরের বাড়ীতে। হুজুর মুখ ধুয়েই উঠতে উঠতে বাঈ মেওয়াফল আর অন্য ফল কেটে নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকত; আমি গরম দুধ, মাখন, মিছরি প্যাড়া এনে নামিয়ে দিতাম। হুজুর খেতেন; সোফিয়া বাঈ বসে খাওয়াতো। সতীরানী মা বাঈকে ভারটা ডেকে দিয়ে গিয়েছিলেন। খেতে খেতে গল্প করতেন। হাসতেন, মস্করা করতেন। আমি তামাক সেজে নলটি রেখে বাইরে গিয়ে বসে থাকতাম। খাওয়ার পর ডাক পড়ত তবলচীর আর সারেঙ্গীদারের। গানের আসর বসত। একটা বাজলে সে আসর ভাঙত। হুজুর স্নান করে খেয়ে উঠে শোবার আগেই বাঈ আবার এসে হাজির হত পানের রেকাবি হাতে। পান-তামাক খেয়ে হুজুর শুতেন। বাঈ প্রথম প্রথম চলে যেত, দিন কয়েক পর থেকেই হুজুর বলেছিলেন—মাথায় হাত বুলিয়ে দাও; ভবানী দিত, পাকাচুল তুলত। অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। না দিলে ঘুম আসবে না।
বাঈ মাথার শিয়রে কুর্সি টেনে নিয়ে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিত। পাকা চুল তুলতে বললে বলত—হুজুর, এখন তুমি ফের নওজোয়ান হয়ে গেছ, এখন কি আর পাকাচুল থাকে?—
হুজুর খুব হাসতেন। এই সময় হুজুর আর একরকম মানুষ হয়ে যেতেন।
***