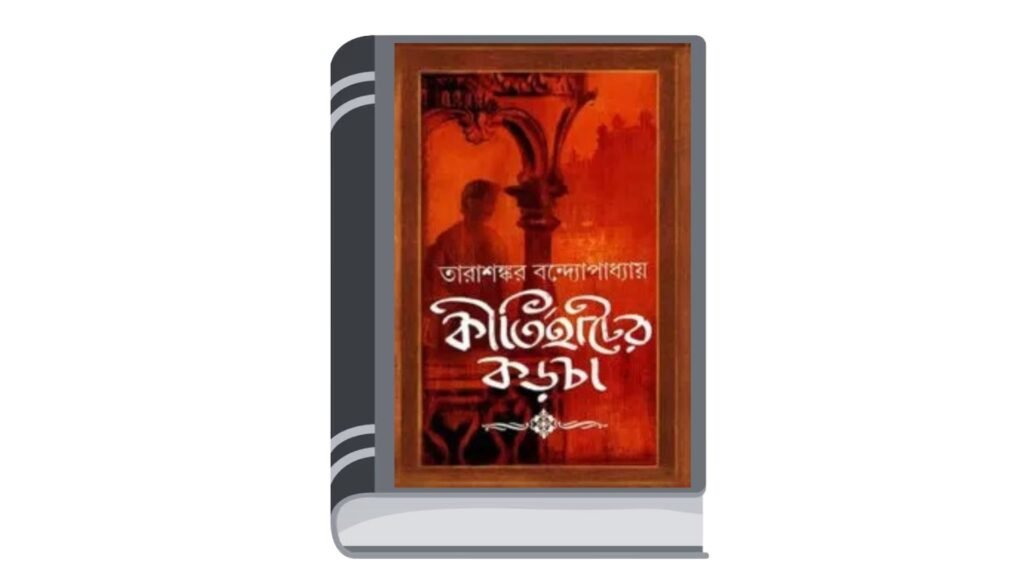কীর্তিহাটের কড়চা – ৩য় খণ্ড – ১৪
১৪
কাশী থেকে রওনা হয়েছিলেন, বিন্ধ্যাচল হয়ে প্রয়াগ। জষ্টি মাসের পনের-ষোল তারিখে। পনের তারিখের শেষ রাত্রে ষোল তারিখের ভোরে। সতীবউরাণী একমাস ব্রত করে বড় দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন; তিনি একটু বল পাবেন—এই বলে অপেক্ষা করা হয়েছিল।
কিন্তু কাশী থেকেই আগের হালচাল সব বদলে গেল। সতীবউরাণী বাসা নিলেন নিজের ঠাকুর ছিল যে বজরায় সেই বজরায়। সেইখানেই তাঁর খাওয়া সেইখানেই শোওয়া। মাত্র তিনবার আসতেন এ বজরায়। একবার চরণোদক দিতে, একবার হুজুরের দিনে খাবার সময়, একবার রাত্রে খাবার সময়। ব’সে থেকে খাইয়ে হুজুরকে শুইয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে হুজুর ঘুমিয়ে পড়লে তবে চলে যেতেন।
বলেছিলেন—তীর্থ শেষ করে ফিরে আবার আগের মতন হবে সব। তীর্থে যাচ্ছেন, ভগবান দর্শন করতে চলেছেন, এ সময় একমন হয়ে যেতে হবে। ওই চিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তা করলে কি ভগবানের দর্শন মেলে?
বলতেন—যে যে-চিন্তা নিয়ে যায়, তীর্থের মন্দিরে দেবতার মূর্তির বদলে সে তাই দেখে। দেবতা দেখতে পায় না!
হুজুর মুখে কিছু বলেন নি, কিন্তু মেজাজ তাঁর আরো গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। বলেছিলেন—বেশ, তাই হবে। তোমার যখন তাই ইচ্ছে, তখন তাই হবে।
মহেন্দ্র বলেছিল—হুজুরের বজরার কামরায় আমি শোব এই ব্যবস্থা করেছিলেন রাণীমা। আমি শুতাম।
প্রয়াগ থেকে বজরা ঢুকল যমুনায়। বরাবর এসে উঠল মথুরায়, তারপর বৃন্দাবনে। বৃন্দাবনে দশদিন থেকে ফিরে এসে উঠলেন আগ্রায়। তবে মাসিমারা থেকে গেলেন বৃন্দাবনে। আগ্রায় দেবদেবতা নেই, সেখানে থেকে কি করবেন? আগ্রায় বাড়ী ভাড়া করে দশদিন পর হুজুর রাণীমা, সোফিবাঈ আর লোকজনকে নিয়ে গিয়ে আগ্রায় উঠলেন।
রাণীমায়ের শরীর তখন আরো খারাপ হয়েছে। রোগা হয়ে গেছেন। আর মনে মনে কি ভাবেন, যেন মাটির মানুষই নন। খেতে কিছু পারেন না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অরুচি।
মহেন্দ্র মাথা চুলকে রত্নেশ্বর রায়কে বলেছিল —মাসিমারা ফিসফাস্ গুজগুজ করছিলেন। মানে।
রত্নেশ্বর বলেছিলেন—হুঁ।
মহেন্দ্র এসব কথা রত্নেশ্বর রায়কে বলেছিল তীর্থ থেকে ফিরে আসার পর। সে প্রায় এক বছর পর। তীর্থপর্যটনে লেগেছিল ছ’ সাত মাস, ছ’ সাত মাস পর তাঁরা ফিরে এসেছিলেন কাশীতে। কাশীতেই একটি কন্যাসন্তান প্রসব করে ভবানী দেবী মারা যান।
রত্নেশ্বর মোটামুটি ঘটনাগুলি জানতেন, তাই বলেছিলেন—হুঁ। বীরেশ্বর রায়ের মাসিমা এবং অন্যান্য প্রবীণারা কী কানাঘুষো করেছিলেন, তা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই বলেছিলেন—হুঁ। কথাটা কিন্তু কেউ প্রকাশ্যে বলতে ভরসা পায় নি। তার কারণ ভবানী দেবী। ভবানী দেবী বারো বছর পর স্বামীর ঘরে ফিরে এসেও ঠিক সংসারী হন নি। এবং কালটা সে-কাল! কুড়ি-বাইশ বছর পর এমন ধর্মপরায়ণা পূজারিণীর মত মেয়ে সন্তানবতী হয়েছে, এটা যেন প্রবীণাদের কাছে একটু কেমন ভোগলিপ্সা অপবাদের মত মনে হয়েছিল। ভবানী দেবীর নিজের কাছেও সেটা অপরাধ বলে মনে হয়েছিল।
সুরেশ্বর বললে—সুলতা, প্রমাণ সঠিক মানে লিখিত প্রমাণ আমি পাইনি। তবে আমার বিশ্বাস—তাই। কীর্তিহাটে সেদিন রাত্রে রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রী পড়তে পড়তে আমি যেন চোখে দেখতে পেয়েছিলাম বিশীর্ণা ভবানী দেবীকে। মুখে চোখে তাঁর অপরাধবোধের ছাপ। তিনি যেন মনে মনে বলছিলেন —“একি করলি মা! এ কি লজ্জায় ফেললি। সংসারে ফিরে আসার জন্যে কি এই শাস্তি দিলি!”
আর রাজকুমারী রাণীবউ কাত্যায়নী দেবীর মাসতুতো বোন বৃদ্ধা নিস্তারিণী দেবীর ফিস্-ফাস্ কথাগুলিও যেন কানে শুনেছিলাম—ছি-ছি মা, এ কি লজ্জা! এতকাল পর! পুষ্যিবেটা একুশ পার হয়ে পড়েছে বাইশে; বউ এসেছে ঘরে, কোনোদিন ডাকে চিঠি আসবে ম্যানেজার নিখবে-রত্নেশ্বরের সাহেব শ্বশুর লিখবে নাতবউয়ের সন্তান হবে! তা না। এখান থেকে খবর যাবে চিঠিতে। নিখবে কি ক’রে গো!
আর একজন বলেছিলেন—তা বীরেশ্বর আমাদের পারবে। দিব্যি পারবে। আগেকার কথা তো ঢাকা নেই। এখন এই দেখ না, তীর্থে এসেছে, সঙ্গে বাঈ নিয়ে এসেছে।
নিস্তারিণী বলেছিলেন—এইবারে আগুন লাগবে দিদি। বাপবেটায় মানে পুষ্যিবেটায় আর বাপের বিষয় নিয়ে লাঠালাঠি হবে। ছেলে আর হবে না এই বলে সব পুষ্যিবেটাকে দানপত্র করে দিয়ে এল। এখন? এখন তো মায়ের, নিজের ছেলে আসবে কোলে! সে কোথা দাঁড়াবে? কি মতিচ্ছন্ন মা! দানপত্তর ক’রে দিলি কেন?
সুরেশ্বর বললে—এ কথাগুলির আভাস আছে রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীতে। তাঁর ডায়রীতে শ্রাবণ মাসের আট তারিখে তিনি লিখেছেন—“আজ আগ্রা হইতে পিতৃদেবের পত্র পাইয়া স্তম্ভিত হইলাম। মাতৃদেবী এত দীর্ঘকাল-একুশ বৎসর পর আবার সন্তান-সম্ভবা হইয়াছেন। বুঝিতে পারিলাম মনুষ্য যতই এবং যেমনি সঙ্কল্প করুক, যত নিষ্ঠার সঙ্গেই ধর্মাচরণ করুক, তাহার প্রবৃত্তির কদাপি পূর্ণ নিবৃত্তি হয় না। পিতা কিছুকাল পূর্ব পর্যন্তও মৃদু হইলেও পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত ছিলেন। তিনি সুস্থ হইবামাত্র আবার ভোগলালসার কাছে পরাজিত হইয়াছেন। কিন্তু আমার নানা চিন্তা হইতেছে। পিতা তাঁহার সম্পত্তি আমাকে দানপত্র করিয়া অর্পণ করিয়াছেন। লোকচক্ষে আমি স্বর্গীয় সোমেশ্বর রায়ের দৌহিত্র হিসাবে তাঁহার সম্পত্তির অর্ধেক অংশের মালিক হইলেও প্রকৃতপক্ষে ষোল আনা সম্পত্তির মালিক তিনি। আমি অবশ্য ইচ্ছা করিলে এই অর্ধেক অংশ নিজস্ব বলিয়া দাবি করিতে পারি। এবং আমার বিশ্বাস পিতৃদেব ও বিষয়ে কোন দাবি করিবেন না। করিতে পারিবেন না। কিন্তু আমার পক্ষে ন্যায় কি হইবে? চিঠিখানা ম্যানেজারকে দেখাইলাম। তিনিও এই কথাগুলিই বলিলেন। অবশ্য দৌহিত্র হিসাবে আমার অংশের কোন কথাই তুলিলেন না। এবং বাড়ীতে এই পত্র সরস্বতীবউও দেখিল। পত্র পাঠ করিয়া সে আমার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপকরতঃ বলিল—এখন কি হইবে? আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কিসের কি হইবে?
সে বলিল-সম্পত্তির?
—পুত্রসন্তান অর্থাৎ ভ্রাতা হইলে তাহার সহিত সমভাগে ভাগ করিয়া লইব। ভগ্নী হইলে প্রচুর খরচপত্র করিয়া উচ্চবংশে তাহার বিবাহ দিব।
সরস্বতীবউ চুপ করিয়া রহিল। মনে হইল আমার কথা তাঁহার মনঃপুত হইল না। আমি বলিলাম—ইহাই কর্তব্য এবং ধর্ম নহে কি?
সে বলিল—না, আমি তাহা মনে করি না। শ্বশুরমহাশয় তোমাকে যে সম্পত্তি দান করিয়াছেন, তাহা ইচ্ছা করিলে তুমি অবশ্যই দিতে পার। কিন্তু জমিদারী সম্পত্তি, বসতবাটী ভাগ হইলেই মাটি হইয়া যায়। তাহার আবার দাম কি? তা ছাড়া শ্বশুরমহাশয়ের কলিকাতার সম্পত্তি তো কম নয়। শুনিয়াছি কয়েক লক্ষ টাকা ব্যবসায়ে খাটিতেছে এবং গোকুলের কৃষ্ণের মত দিনে দিনে বর্ধিত হইতেছে। কলিকাতার বাড়ীতে তোমার ভাগ নাই। ও বাড়ী দাদাশ্বশুর সোমেশ্বর রায় দৌহিত্র হিসাবে তোমাকে দেন নাই। কলিকাতার তেজারতি ইত্যাদিও নয়। সে-সব তো সোনা। এই জমিদারী তাহার কাছে মাটি।
কথায় বাধা পড়িল। অঞ্জনা আসিয়া প্রবেশ করিল। আমি কহিলাম—থাক এখন এসব কথা। সে-সব অনেক দূরের ব্যাপার। এক্ষণে চুপ কর। অঞ্জনা আসিতেছে।”
সুরেশ্বর বললে—কোথা থেকে কোথায় এসে পড়লাম সুলতা! বলছিলাম বীরেশ্বর রায় আর ভবানী দেবীর রায়বাড়ীর রঙ্গমঞ্চ থেকে প্রস্থানের কথা। এসে পড়লাম রত্নেশ্বর রায়ের কথায় কীর্তিহাটের বাড়ীতে। ফিরে আবার সেই কথাই বলি।
আগ্রাতেই প্রথম কবিরাজ এবং ডাক্তার দেখিয়ে বীরেশ্বর রায় জানতে পারলেন যে ভবানী দেবী আবার সন্তানসম্ভবা।
মহেন্দ্র খানসামা রত্নেশ্বর রায়কে বলেছিল—সেদিন রাত্রে রাণীমায়ের সঙ্গে হুজুরের কথা কাটাকাটি হয়েছিল।
রত্নেশ্বর জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কি কথা কাটাকাটি?
মহেন্দ্র চুপ করে থেকেছিল—জবাব দেয় নি।
রত্নেশ্বর রায় ডায়রীতে লিখেছেন—মহেন্দ্রকে দুই-তিনবার জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর না পাইয়া ধমক দিয়া প্রশ্ন করিলাম —কি কথা হইয়াছিল বল। বলিতেই হইবে।
মহেন্দ্র মুখ নিচু করিয়া বলিল—সতীবউরাণী সংবাদ শুনিয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতেছিলেন। হুজুর গম্ভীর মুখে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—কাঁদিতেছ কেন?
ভবানী দেবী বলিয়াছিলেন—এ তুমি কি করিলে?
হুজুর বলিয়াছিলেন—কেন কি হইয়াছে?
—কি হইয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমার ব্রত, ধর্মাচরণ সব পণ্ড হইল, আমার লজ্জার সীমা রহিল না। রত্নেশ্বরের সম্মুখে আমি মুখ তুলিয়া কথা বলিব কি প্রকারে? ইহকালের জন্য আমার পরকাল নষ্ট হইল। জীবনে মাকে ডাকিবার সময় পাইব না। মমতার পাঁকে আবদ্ধ হইয়া ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিব, মায়ের মুখ ভুলিয়া যাইব, আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ কি হইয়াছে। তুমি জান, আমার জীবন ভোগের জীবন নয়। একবার বালিকা বয়সে যখন সমুদয় বৃত্তান্ত জ্ঞাত ছিলাম না তখন তোমাকে দেখিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া বিবাহে সম্মতি দিয়াছিলাম। তাহার ফল কি হইয়াছিল তুমি তো জান! নিজে তুমি কত দুঃখ ভোগ করিয়াছ ভাবিয়া দেখ! বারো বৎসর পর তোমার জীবনসংশয় অসুখের সময় আবার আমি ফিরিয়াছিলাম। সম্ভবত ভুল করিয়াছিলাম। তোমাকে তো বারবার বলিয়াছিলাম ঐসকল কথা।
হুজুর বলিয়াছিলেন—ভুল আমারও হইয়াছিল সতীবউ। তোমাকে বিবাহ করা আমার ভুল হইয়াছিল। তাহার পর আমার জীবনসংশয়ের সময় তুমি ফিরিয়া আসিলে আমার সকল দুঃখ সকল যন্ত্রণার উপশম হইল বলিয়া তোমাকে আঁকড়াইয়া ধরা আমার ভুল হইয়াছিল। আমার বাঁচিতে চাওয়া—বাঁচা ভুল হইয়াছে। তোমাকে লইয়া সুখে কালাতিপাত করিব কল্পনা করা ভুল হইয়াছে। চিকিৎসায় এবং পশ্চিম ভ্রমণে জলবাতাসের গুণে নূতন জীবন লাভ করিয়া জীবন যৌবন ফিরিয়া পাওয়া ভুল হইয়াছে। আমার ভাবা ভুল হইয়াছে—তুমি একান্ত করিয়া আমার। আমার ভাবা ভুল হইয়াছে—আমিই তোমার একমাত্র কাম্য! সবই ভুল হইয়াছে ভবানী, সবই ভুল হইয়াছে!
সতীরাণী মা কেমন হইয়া গিয়াছিলেন, তিনি শুধু বিহ্বলের মত হুজুরের দিকে তাকাইয়া ছিলেন, একটি বাক্য তাঁহার মুখ দিয়া নির্গত হয় নাই।
হুজুর বলিয়া গিয়াছিলেন—বলিতে পার সতীবউ, দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ ছার স্বয়ং মহেশ্বরের সন্তান হইয়াছে বলিয়া তাহারা কি অধার্মিক? ব্রহ্মার ঔরসজাত পুত্র নাই, তাঁহার মানসপুত্র আছে। পূর্ণব্রহ্মের অবতার রামচন্দ্রের পুত্র হইয়াছে, ভগবান কৃষ্ণের সন্তান হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা কি ধর্মভ্রষ্ট? বল—বল। তুমি বহু শাস্ত্র পাঠ করিয়াছ, তুমি বল—তোমার উত্তর আমি শুনিতে চাই। বল—বশিষ্ঠের শতপুত্র ছিল বলিয়া কি তাঁহার পত্নীর পরকাল নষ্ট হইয়াছে? সীতার পুত্র লবকুশ, সাবিত্রী শতপুত্রের বর লইয়া স্বামীকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন বলিয়া কি তাঁহারা নরকস্থ হইয়াছেন? বল—শুনি!
মহেন্দ্র বলেছিল রত্নেশ্বর রায়কে–হুজুর, আমি হুজুরের পিছনে পিছনে আসছিলাম, হুজুর রাণীমার ঘরে ঢুকলেন আমিও সঙ্গে সঙ্গেই ঢুকেছিলাম, কিন্তু রাণীমাকে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে দেখে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। তারপরই কথা আরম্ভ হল। রাণীমায়ের কথা শুনতে শুনতে মনে হ’ল আমি সরে যাই। কিন্তু হুজুরের গলা তো জানেন, আর তিনি ঠাণ্ডা গলাতেও কথা বলছিলেন না। ঘরখানা গগম্ করছিল। তার আওয়াজ পেয়ে অন্য চাকরবাকরেরা ঝিয়েরা এসে বারান্দায় উঁকি মারছিল। আমি কি করব? রাণীমায়ের ঘরের দরজাটা টেনে দিয়ে আমি দরজা আগলে দাঁড়িয়ে রইলাম। হাতের ইশারায় সকলকে চলে যেতে বললাম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনতে হল। শুনলাম।
তারপরই হুজুর ডাকলেন—মহিন্দর, মহিন্দর!
আমি ঘরে ঢুকে দাঁড়ালাম। দেখলাম—হুজুর রাণীমায়ের বিছানার পাশে বসে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন।
আমাকে দেখে বললেন—জল, জল আন মহিন্দর, জল। আর পাখা!
মা মূর্ছা গিয়েছেন।
মাথায় মুখে জলের ছিটে দিয়ে হুজুর ডাকছিলেন—রাণীমার নাম ধ’রে। তাঁর হাত কাঁপছে। হুজুর, আমি চেঁচিয়ে দামিনী ঝিকে ডাকলাম—সে ছুটে এল।
জ্ঞান অল্পক্ষণ পরেই হল। জ্ঞান হয়ে আমাদের সকলকে দেখে একটু হেসে মা বললেন—থাক্—থাক্। কেমন মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল। এখন বেশ সুস্থ হয়েছি। থাক্ আর বাতাস করতে হবে না।
হুজুরকে বললেন—যাও, যাও, তুমি এখানে থেকো না। আমার কিছু হয়নি। মাথার শিয়রে বসে থাকতে হবে না। যাও।
—তারপর সুলতা, সুরেশ্বর বললে—আর কোনোদিন কোন এমন কথা হয় নি। এর-পর থেকে নাকি ভবানী দেবী ধীরে ধীরে সেরে উঠেছিলেন। নানান রকম খাবারের ব্যবস্থা হয়েছিল। সকালবেলা থেকে বেদানার রস, আঙুরের রস, বাদামের শরবৎ, পেস্তা, কিসমিস, তার সঙ্গে ঘি দুধ প্রচুর পরিমাণে খেতেন তিনি।
আগ্রায় আষাঢ় মাস থেকে প্রচণ্ড গরম আরম্ভ হয়েছিল। তাই আগ্রা থেকে বজরায় দিল্লী পৌঁছে, সেখান থেকে পাল্কী ঘোড়া, বয়েল গাড়ীতে হরিদ্বারে গিয়েছিলেন বীরেশ্বর রায়।
দিল্লীতে এসে সোফিয়া বাঈজীর বিদায় নেওয়ার কথা। চলে যাবেন আজমীঢ়। চিরজীবনের জন্যই যাবার কথা। কিন্তু আজমীঢ় যাওয়া তাঁর হয় নি। যেতে দেন নি ভবানী দেবী।
হুজুরের যত্ন ভাল হবে না। তা ছাড়া তিনি বলেছিলেন-এবার এসময় আমার দরকার আছে সোফি বাঈ।
সোফি বাঈ আগ্রা থেকেই নীরব হয়ে গিয়েছিল। চুপচাপই থাকত। সে সেলাম করে বলেছিল—আমাকে আপনার দরকার আছে হুজুরাইন?
—হাঁ, দরকার আছে সোফি। এতদিন তুমি তোমার হুজুরকে গান শুনিয়েছ, এবার আমাকে শোনাবে। ভজন, স্রিফ ভজন!
সোফি হেসে বলেছিল—বেশ। তাই হবে! আমি তো একলা হুজুরের বাঁদী নই। আমি আপনারও বাঁদী।
ভবানী দেবী বলেছিলেন—আরো আছে সোফি বাঈ। তুমি আমার পিতাজীর ধরম বেটী। তাঁর শেষ কাজ আমি করতে পারি নি। সে করেছ তুমি। তুমি আমার বহেন। তাঁর কাছে তুমি শেষ শিক্ষা নিয়েছ, দীক্ষা নিয়েছ। ভজন শিখেছ। সেই ভজন আমাকে শোনাবে। তা ছাড়া হুজুরের তোমার দিল খুশ রাখবে কে? আমি তো আর পারব না! তুমি ছুটি নিলে তার ব্যবস্থা তো করতে হবে আমাকে। কিন্তু আমাকেই যে ছুটি নিতে হবে।
মহেন্দ্র সেদিনও কাছে ছিল, ওঁদের কাজ করছিল। রত্নেশ্বরকে সে যা বলেছিল তা তাঁর ডায়রীতে আছে।
“মহেন্দ্রের কথাগুলি শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। মহেন্দ্ৰ বলিল—আমার মাতৃদেবীর কথা শুনিয়া সোফি বাঈ নাকি চকিত হইয়া বলিয়াছিল—
—ছুট্টি? এ কি বাত্ বলছেন দিদিজী?
—হাঁ। ছুট্টি তো নিতে হবে ভাই। এই অবস্থায় কি আমি তাঁর সেবা করতে পারি। আমার কি সে বল আছে? না হুজুর তোমার আমাকে কাজ করতে দেবেন?
সোফি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—তুমি আমাকে ভুলাচ্ছ দিদিজী?
হেসে উঠেছিলেন ভবানী দেবী।
সোফি জিজ্ঞাসা করেছিল—বেশ, কত দিনে ছুটি মিলবে আমার?
—খুদা মালুম সোফি!
রত্নেশ্বর রায় ডায়রীতে লিখেছেন-”আমার ভগবতীর কৃপাধন্যা জননী তাহা হইলে সব অবগত হইয়াছিলেন।”
কার্তিকের প্রথমে হরিদ্বার থেকে দিল্লী ফিরে সেখানে দিন দশেক থেকে ওঁরা ফিরেছিলেন কাশী।
সেও ভবানী দেবীর ইচ্ছায় এবং আগ্রহে। সন্তান কাশীতে হবে।
ছেলে হ’লে নাম রাখবেন বিশ্বেশ্বর। কন্যা হ’লে নাম রাখবেন—অন্নপূর্ণা!
পুত্র নয়—একটি কন্যা প্রসব করেছিলেন ভবানী দেবী।
বিমলাকান্ত কাশীতে সুপরিচিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের পর কোম্পানীর সাহেব মেমসাহেবদের বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলেন বলে তাঁর পদোন্নতিও হয়েছিল। তখন তিনি কালেক্টরেটের অ্যাকাউন্ট্যান্ট হয়েছেন। ডাক্তার দাই এগুলি অর্থাৎ আঁতুড়ে থাকবার লোক ইত্যাদির সব ব্যবস্থা তিনিই করেছিলেন। কেউই বিশেষ আশঙ্কা করেন নি। তবে মাসিমারা আশঙ্কা করেছিলেন। এতকাল পরে সন্তান হবে। তার উপর ভবানী দেবীর শরীর আবার যেন কিছু খারাপ হয়ে পড়েছিল—শেষের দু’মাস।
সুরেশ্বর বললে—কথাটা কাশীতে ফিরে আসার পর থেকেই গুছিয়ে বলি সুলতা। ভবানী দেবীর বৃত্তান্ত রায়বাড়ীর সর্বাঙ্গে সর্বকর্মে বোধহয় জড়িয়ে আছে।
ভবানী দেবীও কাশীতে এসে আবার যেন বদলে গেছেন। প্রথম তিন মাস আগ্রা পর্যন্ত তিনি মনে মুহ্যমানা এবং দেহে শীর্ণা হয়েছিলেন। কিন্তু আগ্রা থেকে স্বামীর সঙ্গে ওই কথাবার্তার পর হয়েছিলেন অন্য মানুষ। হাসি আনন্দ যেন তাঁর জীবনের পাত্র থেকে উপচে পড়ত। সোফির কাছে গান শুনতেন। স্বামীর খাওয়া-দাওয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের এতটুকু ত্রুটি হতে দিতেন না। কিন্তু কাশী ফিরে আট মাসের শেষ থেকে তিনি আবার বদলালেন।
স্বামীকে বললেন—এবার আমাকে ছুটি দাও। এই শরীর নিয়ে আমি যেমন দেখাশুনো করতাম তা আর করতে পারব না। হাঁটতে ফিরতেও আমার কষ্ট হয়।
মহেন্দ্র রত্নেশ্বর রায়কে বলেছিল—হুজুর বলেছিলেন—না—না। বেশী হাঁটাহাঁটি তুমি করো না। বিশ্রাম নাও। আমার জন্যে ভেবো না। মহেন্দ্র আছে। তা ছাড়া সোফি রয়েছে। আর মন্দির-টন্দিরে যাওয়াও বন্ধ কর। হাঁটাহাঁটি তোমার ওখানেই বেশী হয়। আর ওই উপোসগুলি। ওগুলিও এখন বাদ দেওয়া দরকার। নেহাৎ কোন পর্ব হলে—কি একান্ত ইচ্ছে হলে এক-একদিন—
বাধা দিয়ে ভবানী দেবী নাকি মাথার ঘোমটাটা একটু টেনে দিয়ে হেসে বলেছিলেন—না, তাও আর যাব না। স্নানজল নির্মাল্য আসবে, তাতেই হবে।
সুরেশ্বর বললে—ভবানী দেবী এই বয়সে তাঁর এই অবস্থান্তরে লজ্জিত হয়েছিলেন। এবং মনে মনে ক্ষুণ্নও হয়েছিলেন এর জন্যে। সম্ভবত স্বামীর কাছে ফিরে এসেও তিনি দেহসম্পর্করহিত একটি দাম্পত্য জীবনের কল্পনা করেছিলেন। প্রথম প্রায় একবছর বীরেশ্বর রায় আংশিক পক্ষাঘাতে রোগীর মতই জীবনযাপন করেছিলেন। সুতরাং এ নিয়ে কোন দ্বন্দ্ব স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হয় নি। কিন্তু এক বৎসর নিয়ম পালন করে সুচিকিৎসায় ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠেও যেটুকু রোগ অবশিষ্ট ছিল তা থেকেও এই চেঞ্জে যাওয়ার ফলে পরিপূর্ণ রূপে সুস্থ হয়ে উঠেই সহজ এবং স্বাভাবিক দাম্পত্যজীবন ফিরে পেতে চাইবেন এ অত্যন্ত স্বাভাবিক। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর ভোগী মানুষ। দুর্বল ভোগী নয়—সবল ভোগী তিনি। কিন্তু ভবানী দেবী তাঁর বিপরীত। তিনি বারো বৎসর ব্রত পালনের পর স্বামীর রোগশয্যায় ফিরে এসেছিলেন; এবং স্বামী তাঁর পুণ্যেই বেঁচেছেন এই বিশ্বাসবশে আরো গভীরভাবে জড়িয়ে ধরেছিলেন তাঁর তপস্যাকে। তাঁর স্বপ্নভঙ্গ হল-বীরেশ্বর রায়েরও স্বপ্নভঙ্গ হল।
ভবানী দেবী সন্তান প্রসবের দিন গণনা করে ঘরের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখলেন। মন্দিরে তিনি যেতেন না তাঁর দৈহিক অবস্থান্তরের জন্য, কিন্তু ঘরের মধ্যে পূজা পাঠ নিয়েই থাকতেন। স্বামীর কাছে আসতেন দুবার। সকাল এবং সন্ধ্যায়। দুবেলা দুটি প্রণাম করে দুচারটি কথাবার্তা বলে আপনার ঘরে চলে যেতেন।
একঘরে শোওয়া বন্ধ হয়েছিল। প্রথম কাশীতে আসবার পথে, কাশী পৌঁছুবার ঠিক আগের দিন থেকে। কাশীতে এসে থেকেই সেই যে একমাস সারাদিন উপোস করে থাকতেন, ভোরে উঠে কাশীর ভিতরে বিমলাকান্তের বাড়ীর পাশের বাড়ীতে এসে সারাদিন পূজা অর্চনা করতেন, তারপর সন্ধ্যায় আরতি দেখে বাড়ী ফিরতেন—তখন থেকে।
ব্রত উদ্যাপনের পরও পনের দিন কাশীতে ছিলেন—তখনো সেই নিয়ম ভাঙেন নি। তারপর সারা তীর্থ ঘোরার চার-পাঁচ মাস সেই নিয়মই বজায় রেখেছিলেন। আগ্রাতে সন্তানসম্ভবা হয়েছেন এই কথাটা যখন ডাক্তার কবিরাজে বলে গেল, তখন স্বামী-স্ত্রীতে যে কথা কাটাকাটি হয়েছিল—যার কথা একটু আগেই তোমাকে বলেছি সুলতা—যার পর ভবানী দেবী স্বামীর কাছে নিজেকে সমর্পণ করলেও এই নিয়মটুকু ভাঙেন নি।
তবে একটা নিয়ম নতুন করেছিলেন। হরিদ্বার থেকে ফিরে কাশী ফেরা পর্যন্ত সোফি বাঈ থাকত স্বতন্ত্রভাবে, জলপথে স্বতন্ত্র বজরায়, কাশীতে আগ্রায় হরিদ্বারে স্বতন্ত্র কুঠিতে; সেখান থেকে সে আসতো যেতো নিয়মমাফিক, সকালে জলখাবার সময় ফল কেটে আনত, পান আনত, গান শোনাতো, দুপুরে খাওয়ার সময় এসে দূরে বসে থাকত; বড় রায় হুজুর শুলে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে কথা বলে মনোরঞ্জন ক’রে ঘুম পাড়াতো; আবার সন্ধের সময় গানের মজলিশে আসত। হরিদ্বার থেকে সন্ধের মজলিশও বসত বড়রায়বাহাদুরের শোবার ঘরে, সেখানে ভবানী দেবী থাকতেন। তারপর সোফি বাঈ চলে যেত। এবার কাশীতে ফিরে ভবানী দেবী বললেন —সোফি থাকবে এই বাড়ীতেই, দোতলায়। ভবানী দেবীর কামরা এবং বড় হুজুরের কামরা একেবারে পূব দিকে, সোফির জন্য নির্দিষ্ট হল একেবারে পশ্চিম দিকের কামরা। আর বদল হল হুজুরের সঙ্গে ভবানী দেবীর কামরার। একেবারে পূর্বদিকের কামরাখানা ছিল সর্বোৎকৃষ্ট—কামরার পূর্বের জানালার নীচেই গঙ্গাও এবং দক্ষিণদিকের জানালা খুললে অবারিত দক্ষিণই শুধু পাওয়া যায় না, গঙ্গা খানিকটা পাওয়া যায়। রায়হুজুরকে দিলেন তার পাশের ঘরখানা, সেখানায় প্রথমবার তিনি থাকতেন।
সুরেশ্বর বললে-তোমার কি মনে হবে বা হচ্ছে তা আমি জানি না সুলতা, তবে আমার মনে হয়েছে বা এখনো আমার তাই বিশ্বাস যে ভবানী দেবীর ওই নতুন ব্যবস্থার মধ্যেই তাঁর নিজের ভবিষ্যৎ তিনি নিজে নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় দেহত্যাগের ব্যবস্থা করেছিলেন বলে আমাদের রায়বাড়ীতে একটা প্রবাদ আজও রয়ে গেছে। মেজঠাকুমা বলতেন—পুণ্যবতীর কাজ ফুরলো, কিন্তু যাই যাই করেও স্বামীর প্রতি মমতায় যেতে পারছিলেন না; তাঁর ইষ্ট তাঁকে সন্তানধারণের লজ্জা দিয়ে চৈতন্য দিলেন-বললেন—বাঁচবি আর? বাঁচতে হলে, এই সংসারপঙ্কে ডুবতে হবে। মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছিস, ভাগ্য তোর সধবার ভাগ্য, ভাগ্যের ফলফুল ধরতে হবে। তা আমার দিদিশাশুড়ি প্রথম নাকি স্বপ্নে বলেছিলেন-মা, আমি স্বামীকে কাছে পেয়েও সে ব্রত পালনের ধর্মকে ধরে থাকব। কিছুদিন সংসার আমাকে ভোগ করতে দাও। ইষ্টদেবী বলেছিলেন—’বেশ তাই কর।’ বলে হেসে মিলিয়ে গিয়েছিলেন। তা না-হলে নাকি স্বামী বেঁচে উঠলেই তাঁর যাবার কথা ছিল। তা একবছর পার হয়ে দু বছরের বছরেই থাকার মাশুল দিতে হল। সধবা মেয়ে, ফল ধরতে হল। তখন সতীবউয়ের চোখ খুলল। মনে মনে মাকে ডেকে বললেন—আর নয় মা। ভোগের সাধ আমার মিটেছে। আমাকে এবার পায়ে টেনে নে। মা বললেন-তথাস্তু। সংসারে থাকার যে ফলটি জীবনে ফলেছে, ওই ফল বোঁটা খসে মাটিতে পড়ুক—তখন আসব। নিয়ে যাব।
এই স্বপ্নের কথা কে তৈরি করে চালু করে গিয়েছিল তা জানিনে। সুরেশ্বর বললে—তবে আমার মেজদি আমাকে কথাটা বলেছিলেন এবং আজও পর্যন্ত একথা রারবাড়ীর মেয়েরা প্রায় সবাই জানে এবং বিশ্বাস করে। সে অর্চনাও করে!
সুলতা বললে-তোমার কাছে যা শুনেছি তাতে মনে হয়, সে নিজেই ভবানী দেবী, জন্মান্তরে রায়বাড়ীর ঋণ শোধ করতে এসেছে—একথাও বিশ্বাস করে অর্চনা।
—হ্যাঁ তা বোধহয় করে। আগে ছেলেবেলায় তো করতই। তবে এখন এম-এ পাশ করেছে, এখন সেটা ততটা শক্ত আছে কিনা জানিনে।
সুলতা বললে—ছেলেবেলার বিশ্বাস সহজে মরে না। আমি ব্রাহ্ম ঘরের মেয়ে, আমার ঠাকুরদা’র ঠাকুরদা ঠাকুরদাস পালকে কিছুতেই তোমার আঁকা ছবির মত চেহারায় কল্পনা করতে পারি নে, বিশ্বাস করতে পারিনে। মনে হচ্ছে তুমি জমিদারীর অহঙ্কারে চাষী ঠাকুরদাসকে এমন ক’রে এঁকেছ।
—ঠাকুরদাস পালের যে ছবি আমার আঁকা ছবির মধ্যে রয়েছে, তা কল্পনার ছবি নয় সুলতা। রায়বাহাদুর রত্নেশ্বরের আমলে ফটোগ্রাফের রেওয়াজ হয়েছে। রত্নেশ্বর রায় অনেক ফটোগ্রাফ তুলিয়েছেন—তার মধ্যে চার-পাঁচখানা গ্রুপ ফটো আজও আছে, বিবর্ণ নিশ্চয় হয়েছে, কিন্তু তবুও ঠাকুরদাসকে সবগুলোতেই চেনা যায়। আমি তাকে যেমনটি পেয়েছি তেমনটি এঁকেছি। দেখাতে পারি।
—আমাকে দেবে সেখানা?
সুরেশ্বর হেসে বললে-দেব। কিন্তু কি করবে নিয়ে?
সুলতা বললে-দেওয়ালে ছবি দিয়ে জিনিওলজি তৈরী করব। আমাদের বাড়ীর জীবনের অহঙ্কারকে একটু সংযত করব। যা ছিলাম—যা হইয়াছি। ‘যা হইব’–তার ছবি পারো তো একখানা এঁকে দিয়ো।
—কিন্তু কতদিন পরের ভবিষ্যৎ সেটা বল? চরম ভবিষ্যতের ছবি আঁকতে পারি। সেটা আমি ভবানী দেবীর মত জানি। তার এদিকের যে ভবিষ্যৎটুকু সেটা আমার অজানা। ভবানী দেবী একখানা চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিলেন তাঁর স্বামীকে। তিন মাস পর মাঘ মাসে তিনি একটি কন্যা প্রসব করে মারা যান। কাশীর সিবিল সার্জেন থেকে ভাল ডাক্তারদের ডেকে বীরেশ্বর রায় ডাক্তারের হাট বসিয়ে দিয়েছিলেন। সিবিল লাইনের একজন মেমসাহেব মিডওয়াইফকে এনেছিলেন ডেলিভারীর জন্যে। তিনদিন লেবার পেনের পর ডেলিভারী হল। হ’ল কন্যাসন্তান। তারপর হল ভবানী দেবীর জ্বর। সেই জ্বরে আর তিনদিন পর তিনি মারা গেলেন।
সেদিন তিথি ছিল পুর্ণিমা। মাঘীপূর্ণিমা হিন্দুশাস্ত্রমতে শ্রেষ্ঠ পুণ্যতিথিগুলির মধ্যে একটি। মাঘী পূর্ণিমা, দোল পূর্ণিমা, বৈশাখী পূর্ণিমা
মৃত্যুর পর ভবানী দেবীর হাতবাক্স থেকে চিঠিখানা পেয়েছিলেন বীরেশ্বর রায়।
সুরেশ্বর বললে—সুলতা, রায়বাড়ীর পুরনো কাগজ ঘেঁটে অনেক মূল্যবান দলিল পেয়েছি; বীরেশ্বর রায়ের স্মরণীয় ঘটনাপঞ্জী পেয়েছি; রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের তিরিশ বছরের ডায়রী পেয়েছি; দেবোত্তরের সিন্ধুকের মধ্যে তাড়াবাঁধা চিঠির মধ্যে সোমেশ্বর রায়—রাণী কাত্যায়নীর প্রেমপত্র পেয়েছি; বীরেশ্বর রায়কে শ্যামাকান্তের গোপন সাধনার কথা লিখে যে পত্র ভবানী দেবী লিখেছিলেন তাও পেয়েছি। চন্দন-কাঠের বাক্সে কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্যের কীর্তিহাটের পাঁচালী পেয়েছি, কিন্তু ভবানী দেবীর এই চিঠির মত মূল্যবান আমি আর কিছু পাইনি। চিঠিখানা আমি অহরহ সঙ্গে রাখি। রাত্রে মাথার বালিশের তলায় রেখে শুই। ছবি আঁকবার আগে বা কোন কাজ করবার আগে কপালে ঠেকাই
জামার ভিতরের পকেট থেকে একটি সুদৃশ্য মরক্কো লেদারের নোটকেস বের করে তার ভিতর থেকে একখানি বিবর্ণ কাগজ বের করে সযত্নে ভাঁজ খুলে সামনের টেবিলের উপর সে মেলে ধরলে।
—এই দেখ।
সুলতা দূর থেকেই চিঠিখানার হস্তাক্ষর দেখে বিস্মিত হল। গোটা গোটা সেকালের ছাঁদের হস্তাক্ষর, কিন্তু ভারী সুন্দর। আরো একটা কথা—লেখাগুলি এতটুকু অস্পষ্ট হয় নি। কালি যেন ডগডগ্ করছে। কালি সম্পর্কে বিস্ময় তার ছিল না, কারণ সোসিওলজি সম্পর্কে রিসার্চ করতে গিয়ে অনেক পুরনো পুঁথি সে ঘেঁটেছে। তার মধ্যেও এই কালির দীপ্তি সে লক্ষ্য করেছে। সেকালে এদেশে লোহার কড়াইয়ে নানারকম জিনিস ভিজিয়ে তার কষ থেকে কষের কালি তৈরির কথা সে জানে। একটা উপাদান —হিরাকষের নামও তার মনে আছে।
চিঠিখানার উপর সাগ্রহে সে ঝুঁকে পড়ল। প্রথমেই সম্বোধনটা বড় ভাল লাগল।
***
জন্মজন্মান্তরের পরমারাধ্য প্রিয়তম
স্বামীন্—
দাসীর শেষ প্রণাম নিবেদন করিতেছি, গ্রহণ করুন। শেষমুহূর্তে আমার জ্ঞান থাকিবে না—সেই কারণে আমি প্রণাম এই পত্রে নিবেদন করিয়া রাখিলাম।
সন্তান প্রসব করিয়াই আমার জীবনের পালা সম্বরণ করিতে হইবে, ইহাই দৈবাদেশ। সজ্ঞানে আপনাকে দেখিয়া দেহত্যাগে দুঃখ অনুভব করিব বলিয়াই মার নিকট ইহাই আমি চাহিয়াছিলাম। জানি তুমি ইহা বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু বিশ্বাস করিও—দৈবাদেশ স্বপ্নযোগেই হইয়া থাকে। ইহা বিশ্বাস করিও। তোমাকে কতদিন তো বলিয়াছি, স্বপ্নযোগে মায়ের সঙ্গে আমার কথাবার্তার কথা। বারো বৎসরের ব্রত উদযাপন করিতে আসিয়া—তোমার অসুখের কথা শুনিয়া —ত অসম্পূর্ণ রাখিয়া তোমার শিয়রে আসিয়া বসিয়াছিলাম। মা তোমাকে বাঁচাইলেন। আমাকে বলিলেন—তুই ফিরিয়া আয়। কিন্তু তোমাকে ফিরিয়া পাইয়া যাইতে দুঃখবোধ করিলাম। নয়নযুগল হইতে অশ্রু বিনির্গত হইল; জননী হাসিলেন। বলিলেন—থাকিলে এয়োতী নারীর ফল ভোগ করিতে হইবে! ফল ধারণ করিয়া সৃষ্টির নিয়ম মানিতে হইবে। পতিনিন্দা শুনিয়া সতী দেহত্যাগ করিয়াও শিবের প্রতি এমত আকর্ষণে ফিরিয়া উমা হইয়া গিরিরাজতনয়া হইয়াছিলেন। এবং শিবকে লাভ করিয়া, যিনি নিজেই মহাপ্রকৃতি, তাঁহাকেও ফল ধরিতে হইয়াছে। স্বকীয় অঙ্গের হরিদ্রা হইতে গঠন করা পুতুল জীবিত হইয়া গণেশ হইল অতঃপর কার্তিকেয়। কার্তিকেয়ের জন্য শিব উমার সহিত রতিরঙ্গে মাতিয়াছিলেন।
এ স্বপ্নের কথা তোমার নিকট নিবেদন করিয়াছিলাম। এই দিবস তুমি আমাকে বলিলে—দেখ ভবানী, ইতিপুর্বে তুমি আমাকে অনেক স্বপ্নের কথা বলিয়াছ, আমি এসম্পর্কে কোন প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করি নাই বা উত্তর প্রদান করি নাই। শুনিয়া তোমার তৃপ্তির জন্য কখনো হাস্যসহকারে সন্তোষপ্রকাশ করিয়াছি, কখনো কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছি—কখনো শঙ্কা প্রকাশ করিয়া তুমি যে প্রকার দেবপূজা বা গ্রহস্বস্ত্যয়ন করিতে চাহিয়াছ, তাহাতেই মত দিয়াছি। কিন্তু আজ যে স্বপ্নের কথা বলিতেছ ইহার উত্তর আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মত না দিয়া উপায় নাই। কথাটা হইল কি জান, স্বপ্ন কখনো সত্য হয় না, বা সত্য নহে; দিবাভাগে জাগ্রত অবস্থায় মনুষ্যসকল যে প্রকার চিন্তাভাবনা করিয়া থাকে বা যে সমস্ত ঘটনা সমুদয় সংঘটিত হইয়া থাকে, নিদ্রিত অবস্থার মধ্যেও সেই সকলই কিছুটা এলোমেলো হইয়া বা যেমত তোমার আন্তরিক অভিপ্রায় বা বিশ্বাস তদনুসারে পরিবর্তিত হইয়া স্বপ্ন হইয়া দেখা দেয়।
যেমন ধর—তুমি ক্রমাগতই দেবতার কথা ভাবিয়া থাক। তাহাতে তোমার অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস; সুতরাং তিনিই তোমাকে দেখা দিয়া কথা বলিয়া থাকেন। তোমার মনে হইয়াছে যে—তুমি ব্রত উদযাপন স্থগিত রাখিয়া আমার অসুখের সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিলে এবং আমি পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত হইয়া বাঁচিলাম। তাহাতে তোমার ধারণা হইল যে, এমত কঠিন অসুখ হইতে যখন আমি বাঁচিলাম তখন তাহার মাশুলস্বরূপ তোমার জীবন দিতে হইবে। বা আমার জীবন লাভেই তোমার তপস্যা পূর্ণ হইল-এবার তোমাকে যাইতে হইবে। এবং এতদিন ব্রহ্মচর্য করিয়াছ, তপস্যা করিয়াছ, তাহার ফলে তোমার মনে ধারণা হইয়াছে যে, ইহার পর সন্তান ধারণ করা তোমার পক্ষে পাপ বা শাস্তিস্বরূপ হইবে। সুতরাং এমতপ্রকার স্বপ্ন তুমি দর্শন করিয়াছ।
আমি খুবই আঘাত পাইয়াছিলাম। তাহার কিছুটা তুমি অনুভব করিয়াছিলে। এবং কিছুক্ষণ পর আবার আমাকে ডাকিয়া কাছে বসাইয়া বলিয়াছিলে—ভবানী, আমি ভাবিয়া দেখিলাম আমার কথা ভুল; আমি এতকাল নাস্তিক ছিলাম, সেইমত আচরণ করিয়াছি; সেইহেতু এতবড় দৃষ্টান্তের এবং শিক্ষার পরও মূঢ়ের মত তোমার কথায় প্রতিবাদ করিয়াছি। কিন্তু তুমি চলিয়া গেলে অনেক চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে আমি সত্যই মুঢ় ভ্রান্ত। দেখ, যতবার এমত চিন্তা মনে উদিত হইল ততবারই ঐ কোণে একটা টিকটিকি টকটক করিয়া উঠিল। এবং আরো আশ্চর্যের কথা ততবারই বাহিরে হাঁচির শব্দ শুনিয়াছি। এবং আরো আশ্চর্যের কথা আমার মনের মধ্যেও বারবার মায়ের মূর্তি ভাসিয়া উঠিল।
আমাকে বিশ্বাস করাইবার জন্য তুমি মায়ের একটি বিশেষ পূজা দিতে বলিয়াছিলে। পূজার পর নির্মাল্য ও চরণোদক গ্রহণ করিয়া আমাকে বলিয়াছিলে—এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হইলাম।
সেই রাত্রে তুমি আমাকে বলিয়াছিলে—দেখ ভবানী, একটি শ্যামাসঙ্গীত আছে। আয় মা সাধন সমরে। দেখি মা হারে কি পুত্র হারে। আমাকে গাহিতে বলিয়াছিলে, আমি গীতখানি গাহিলাম, শেষ হইবামাত্র বলিলে-ভবানী, অতঃপর আমরা যতদিন বাঁচিব, ততদিন এবম্প্রকার সাধনসমরই করিব মায়ের সঙ্গে। আমার দেহের তো এমতপ্রকার অবস্থা। এই অবস্থাই আমাকে এই সাধনজীবনে সাহায্য করিবে। আমরা সংসারে যতদিন বাঁচিব ততদিন ব্রহ্মচারী-ব্রহ্মচারিণীর মতোই জীবন যাপন করিব। দেখাই যাউক না কেন—মা হারে না পুত্র হারে?
আমি আশ্বস্ত হইয়াছিলাম। কিছুদিন বেশই ছিলাম-সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াছিলাম তোমার বিশ্বাস এবং আমার বিশ্বাস এক হইয়াছে।
কিন্তু মায়ের বিচিত্র পাকচক্র দেখ, মদীয় পিতৃদেবের সন্ধানের নিমিত্ত সোফিকে আহ্বান করা হইল এবং মা সেটা করাইলেন আমাকে দিয়াই। আমার ডাকে নির্ভয়ে সে আসিল এবং কথাবার্তার পর যখন তাহাকে বিদায় দেওয়া হইল তখন রত্নেশ্বর কথাবার্তাগুলি শুনিয়া এবং সমস্ত বিবরণ জানিয়া সোফিকে সেই তোমাকে গান শুনাইবার জন্য নিযুক্ত করিল। ভয় করিল-সোফি স্বাধীন থাকিলে হয়তো বা কথাটা প্রকাশ করিয়া দিতে পারে। এবং আশ্চর্যের কথা—আমার মনে হইল—আমি বাঁচিলাম, তুমি পুরুষ এবং ভোগী, তোমাকে তুষ্ট করিবার একজন লোক পাইলাম—তাহাকে আড়াল দিয়া আমি বাঁচিব।
তুমি ক্রমশ সুস্থ হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিলে। আমি সোফিকে আরো বেশী করিয়া সামনে আনিলাম। কিন্তু তুমি তাহাকে অবহেলা করিয়া আমাকেই আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে। রত্নেশ্বরকে যজ্ঞ করিয়া গ্রহণ উপলক্ষে তুমি তাহাকে কীর্তিহাট লইয়া যাইতে ইচ্ছুক ছিলে না। কিন্তু আমিই জোর করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম।
তোমার মনে পড়িবে—আমি বলিয়াছিলাম-একনিষ্ঠভাবে সে তোমার মনোরঞ্জন করিয়া তোমার এক ধরনের পত্নীত্ব লাভ করিয়াছে। মহাভারতে মহাত্মা বিদুরের গর্ভধারিণী দাসী ছিলেন। ইহা আমাদের শাস্ত্রে আছে। তুমি কোন উত্তর প্রদান কর নাই। তবু লইয়া যাইতে সম্মতি প্রদান করিয়াছিলে। এই কারণেই তাহাকে আমি সকালে তোমার ফল কাটিয়া আনিবার ভার দিয়াছিলাম। তুমি যত সুস্থ হইতেছিলে তত বেশী করিয়া আমাকে টানিতেছিলে। আমি তোমাকে ছাড়িয়া মরিতে চাহিতেছিলাম না অথচ ভয় হইতেছিল- সাধনসমরে হয়তো হারিয়া যাইব। মনে কর আমরা সন্তানাদির কামনা করি নাই বলিয়া রত্নেশ্বরের অনুকূলে দানপত্র সমাধা করিয়া দিবার পরামর্শ করিয়াছিলাম।
তাহার পর তীর্থযাত্রার পথে গয়া হইতে ফিরিয়া পাটনায় সেদিন সকালে সোফি ছিল না, আমার পূজা শেষ করিতে বিলম্ব হইয়াছিল—তুমি রাগ করিয়াছিলে- তোমার সন্তোষ সাধন করিতে গান গাহিলাম, তুমি পাখোয়াজ সঙ্গত করিয়া উল্লাসে বলিয়া উঠিলে- আমি ভাল হইয়া গিয়াছি। ছড়ি ছাড়িয়া হাঁটিতে লাগিলে, খানিকটা ব্যায়াম আরম্ভ করিলে, আমি সুখী হইলাম, কিন্তু তুমি যখন আমার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করিতে, তখন ভয় পাইতাম। আরো ভয় পাইতাম দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া। আমারও যেন যৌবন ফিরিয়াছে। মাসিমারা বলিলেন—গঙ্গার বাতাসে, পশ্চিমের জলে আমার শরীর সারিতেছে। এবং জানিয়া আশ্চর্যান্বিত হইবে যে এই সময় মা আমাকে আর স্বপ্নে দেখা দেন নাই।
কিন্তু যেদিন তুমি সোফিকে নাচিতে হুকুম করিলে, সেদিন আমি চমকিয়া উঠিলাম। শঙ্কিত হইয়া চিন্তা করিলাম-নাচ দেখিতে শখ হইল কেন? সোফির কটাক্ষ তাহার অঙ্গের হিল্লোল-লীলা দেখিয়া তোমার পরিবর্তন আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম এবং আমার নিজের মধ্যেও কামনা জাগিয়াছিল—ইহা অস্বীকার করিব না।
তাহার পর যাহা হইল তাহা হইয়া গেল। কুশির মুখে গলিত ঘৃতধারা যখন অগ্নিকে আকৃষ্ট করে তখন ঘৃতের ইচ্ছা অনিচ্ছা কিছুই থাকে না সে, আত্মসমর্পণই করে। আমি ক্ষীণ প্রতিবাদ করিতে গিয়াও পারি নাই।
সেইদিন রাত্রে মনে হইল—এ কি হইল। এ কি করিলাম? সাধনসমরে পরাজিত হইলাম। অনেক কাঁদিলাম। শেষরাত্রে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। তখন স্বপ্ন দেখিলাম। মা দেখা দিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন। মাকে বলিলাম- মা আমার দর্প চূর্ণ হইয়াছে। এইবার চরণে স্থান দাও। টানিয়া লও।
মা বলিলেন—সংসারে থাকিতে চাহিয়াছিলে, তাহার ঋণ শোধ কর। তৎপর তোমাকে টানিয়া লইব। মৃত্তিকাবক্ষে বৃক্ষ জন্মে রস শোষণ করে, তাহার ঋণ শোধ হয় ফলদানে। তোমাকেও ফল দিতে হইবে।
কিন্তু তাহাতেও আমি দমিত হই নাই। আমি যেন ফলবতী না হই এই জন্য কাশীতে বিশেষ সঙ্কল্প লইয়া কঠোর ব্রত করিলাম। তোমার নিকট হইতে ক্রমশ দূরে সরিলাম। লোকসমাজে কি করিয়া মুখ দেখাইব ভাবিয়া পাইলাম না। আগ্রায় তোমার সহিত কলহ হইল। তুমি কঠিন কথা বলিলে। তখন সোফির শরণাপন্ন হইলাম। সোফি আমার ভগ্নীতুল্যা। তোমার দিক দিয়াই নয়, আমার বাবার দিক দিয়াও বটে। তাহাকে ডাকিয়া সব খুলিয়া বলিয়া বলিলাম, সোফি তুমি আজমীঢ় যাইও না। তুমি এখানে থাক। আমাকে রক্ষা কর। ভগ্নীর কার্য কর। ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ধর্ম হইলেও তুমি তাহাকে ভজনা করিয়াছ, তাঁহাকেই চাহিয়াছ; আমার বাবার কাছে দীক্ষা লইয়া তুমি ধর্মেও আমাদের ধর্ম পালন করিতেছ। এ জন্মে তুমি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া ক্ষান্ত হও, তুমি নূতন করিয়া তাঁহার মনোহরণ কর। তাঁহাকে টানিয়া লও।
এ সব বৃত্তান্ত তুমি সোফিকে জিজ্ঞাসা করিলেই জ্ঞাত হইবে। সে কখনই মিথ্যা বলিবে না। সে আমার অনুরোধে, আদেশে নূতন করিয়া সাজিল নূতন করিয়া অঙ্গ মার্জনা করিল। বেণী বন্ধন করিল। আমি সেই সুযোগ দিবার জন্য তাহাকে প্রায়ই নৃত্য দেখাইতে আদেশ করিয়াছিলাম।
তুমি আকৃষ্ট হইলে। তাহার নিকট ধরা দিলে। তখন তোমার শরীর নীরোগ, দেহে পূর্বের বল পাইয়াছ, বলিতে কি তোমাকে দেখিয়া আমারই মনে হইত তুমি সেই যৌবনের বীর নব যুবক!
আমি সোফিকে অধিক করিয়া তোমার দিকে ঠেলিয়া দিলাম। কাশীতে আসিয়া সেই কারণেই সোফিকে দোতলায় স্থান দিলাম তোমার সঙ্গে ঘর বদল করিয়া এক পাশের ঘর লইলাম এবং তোমার ঘরে সোফির আসা-যাওয়ার পথের সব সঙ্কোচ ঘুচাইয়া দিলাম।
স্বামিন্ পরম দেবতা, আমি নিশ্চিত জানি আমার সংসার ভোগের অনিবার্য ফল প্রসব করিয়াই আমাকে যাইতে হইবে। আগ্রাতে তুমি অপেক্ষা করিয়া প্রকারান্তরে আমাকে তিরস্কার করিয়াছিলে যে সংসারে মানুষ যাহারা তাহারা যেন দেবী অংশোদ্ভূতা যাহারা তাহাদিগকে বিবাহ না করে। তাহারা বিবাহ করিয়া স্বামীকে সেবা করে, ভালবাসে স্বামীকে পাইবার জন্য নয় দেবতাকে পাইবার জন্য। সংসার করে স্বর্গলোক প্রাপ্তির জন্য। পরজন্মে বা লোকান্তরে তাহারা স্বামীকে কামনা করে না, তাহারা কামনা করে দেবতাকে। বন্ধনে তাহারা আবদ্ধ হয়, বন্ধন হইতে মুক্তি লাভের জন্য।
স্বামিন্, কথাটি আমি মনে মনে অনেক আলোচনা করিয়াছি। কথাটি এক হিসাবে সত্য বটে। কি করিয়া অস্বীকার করিব? কিন্তু এই হিসাবটি তো মায়া-মোহের মিথ্যা হিসাব। ইহাই তো শাস্ত্রোক্ত পথ। তোমার কথাটি ভাল লাগিবে না। কারণ তোমার অনেক বাসনা আছে। আরো অনেক জন্ম তোমাকে পৃথিবীতে আসিতে হইবে। আমার এ জন্মেই মুক্তি নির্দিষ্ট ছিল। সুতরাং ইহাই অবশ্যম্ভাবী। তুমি যেন আর বিবাহ করিও না। আমার স্বার্থের জন্য বলিতেছি না। তোমার স্বার্থের জন্য বলিতেছি। কারণ নিজের শক্তি না বুঝিয়া তুমি সকল সম্পত্তি রত্নেশ্বরকে দান করিয়াছ। বিবাহ করিয়া নূতন সংসার করিলে নিদারুণ অশান্তি ও পুত্রের সঙ্গে কলহ আরম্ভ হইবে। সে কলহে অর্থাৎ মামলা-মোকদ্দমায় রায়বংশের এবং আমার পিতার সাধনভ্রষ্টতার সকল রহস্য প্রকাশ পাইবেই।
এ সম্পর্কে আমি দাদার সঙ্গে কৌশলে আলোচনা করিয়াছি।”
সুলতা এবং সুরেশ্বর এক সঙ্গেই চিঠিখানা পড়ে যাচ্ছিল। সুরেশ্বর স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললে—
ভবানী দেবীর দাদা বিমলাকান্ত; বুঝতে পারছ সুলতা?
সুলতা ঘাড় নেড়ে জানালে, হ্যাঁ, তা সে বুঝেছে।
তারপর পড়ে গেল—
দাদাকে বলিলাম, দাদা, সম্পত্তি তো রত্নেশ্বরকে দানপত্র করা হইয়াছে। এখন যে সন্তান হইবে তাহার কি হইবে?
দাদা বলিলেন—রত্নেশ্বর অবশ্যই তাহাকে তাহার অংশ দিবে। সে তোমার সন্তান। বীরেশ্বরেরই পুত্র। দানপত্র করিয়াছে বলিয়া কি ‘সে অংশ দিব না’ এমন কথা বলিতে পারে?
আমি বলিলাম—দাদা, বিষয় বিষের তুল্য। ইহা দেবতাকেও স্বার্থপর করে! মানুষকে অমানুষ করে।
দাদা বলিলেন—তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। তবুও রত্নেশ্বর তাহা পারিবে না!
আমি বলিলাম—মা কালী তাহাই করুন। বাবা বিশ্বনাথ তাহাকে সেই সুমতিই যেন দেন। কিন্তু আইনটা কি? আইনের বলে পাইতে পারিবে কি?
দাদা বলিলেন—না। দানপত্রের অর্থই হইল যে দানপত্ৰ সহি এবং রেজেস্ট্রী হইবামাত্র সেই মুহূর্ত হইতে গ্রহীতা মালিক হইল। দাতা আর কোনরূপেই তাহা নাকচ করিতে পারিবেন না। তবে অনেক সময় এমন মামলা হইয়া থাকে, দাতা প্রমাণ করিতে চাহেন যে তিনি অসুস্থ, বিকৃতমস্তিষ্ক ছিলেন। তাহা ব্যতীত এ ক্ষেত্রে যদি সকল কথা অর্থাৎ রত্নেশ্বর বিমলার গর্ভজাত আমার পুত্র হিসাবে স্বর্গীয় শ্বশুর মহাশয় সোমেশ্বর রায়ের পৌত্র নহে, সে বীরেশ্বরের ঔরস-জাত পুত্র, কেবলমাত্র বিমলার পুত্র চুরির অপরাধ গোপনের জন্য এমত প্রচার করা হইয়াছিল, তাহা হইলে সবই নাকচ হইয়া যাইবে। দৌহিত্র হিসাবে সোমেশ্বর রায়ের উইলসুত্রে সে যে আট আনার মালিক, তাহার মালিকও বীরেশ্বর হইবেন এবং পোষ্যপুত্র হিসাবে যে আটআনা দান করিয়াছেন, তাহাও নাকচ হইবে। সুতরাং চিন্তা করিও না। এ কার্য রত্নেশ্বরও করিবে না। বীরেশ্বরও করিবে না। তাহাতে আমাদের পিতৃদেবের মর্মান্তিক কথা এবং শ্বশুর মহাশয়ের মনোহরা যোগিনী লইয়া কেলেঙ্কারির কথা সমুদয় প্রকাশ হইয়া যাইবে। সমগ্র দেশে রায়বংশের আর মুখ দেখাইবার যো থাকিবে না।
এই কথা তোমাকেও প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তুমি বলিয়াছিলে, নিশ্চিন্ত থাক। রত্নেশ্বর এমত করিবে না। যদি করে তাহা হইলেও চিন্তা নাই। কলিকাতার বাটী, সম্পত্তি এবং নগদ কারবারের যে টাকা আছে তাহা সমুদয় আমি আমাদের এই সন্তানকে দিব। তাহা ব্যতীত আমার পিতামহের আমল হইতে কিছু হীরা জহরতের সঞ্চয় আছে। আমার পিতৃদেব সে সঞ্চয় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। আমি তাহাতে হাত দিই নাই। মধ্যে মধ্যে দু-চারিখানি কিনিয়াছি। পিতৃদেব এ সঞ্চয় দৌহিত্রকে দেন নাই। আমাকেই দিয়াছিলেন। তাহার মূল্যও অন্তত তিন লক্ষ টাকা। ওই সকল জহরতের মূল্য এখন বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিলাতের লর্ডদের এইসকল রত্নরাজিতে ঝোঁক বাড়িয়াছে। এ সমুদয় হইতে আমি আর একটা কীর্তিহাট এস্টেট গড়িয়া তুলিব।
একটি সন্তানের তাহাতে ব্যবস্থা হইবে। কিন্তু আমার পর বিবাহ করিলে তাহার গর্ভে চার-পাঁচ বা ততোধিক সন্তান জন্মিলে কি করিবে? এবং তাহাদের যিনি জননী হইবেন, তিনিই বা মানিবেন কেন? সন্তানেরাই বা শুনিবে কেন?
তুমি ভাবিও না আমি আমার সন্তানদের স্বার্থহানির কথা চিন্তা করিয়া এ সকল কথা লিখিতেছি। আমি ইহা লিখিতেছি এই বংশ কলঙ্ক প্রকাশ হইয়া যাইবে আশঙ্কায়।
তুমি সোফিয়াকে লইয়া থাকিও। সোফিয়া বাঈজী হইলেও এতকাল ধরিয়া তোমাকে ভজনা করিয়াছে, তোমার প্রতি তাহার প্রেম অতি গভীর। সে আমার মত নয়। সে তোমাকেই চায়, মুক্তি সে চাহে না। সে আজমীঢ় না গিয়া তোমাকে পাইবার আশা পাইয়া ফিরিয়াছে। সে আমারই মত তোমার সেবা করিবে। সম্ভবত অধিক মাত্রায় করিবে।
আমার বক্তব্য শেষ হইয়াছে। কি আর লিখিব? তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া এ জীবনে আমার সকল সাধই পূর্ণ হইয়াছে। তুমি ছাড়া আর কাহারও সহিত বিবাহ হইলে সে আমার বারো বৎসর ব্রতকাল পর্যন্ত বিবাহ না করিয়া থাকিত না। এবং তাহার সংসারে আমার আর স্থান হইত না। এবং ভাগ্যের চক্রান্তে যে সন্দেহ তুমি করিয়াছিলে তাহাই লোকসমাজে প্রচারিত হইয়া আমার ললাটে কলঙ্ক কালিমা লেপিয়া দিত। রত্নেশ্বরের ভাগ্যেও লাঞ্ছনার অন্ত থাকিত না।
আমার অসংখ্য কোটি প্রণাম গ্রহণ করিও। আমাকে হাসিমুখে বিদায় দিও। আমার অপরাধ মার্জনা করিও।
আমার সন্তান বাঁচিলে—বাঁচিবে বলিয়াই মা বলিয়াছেন, এবং সন্তান কন্যাসন্তান হইবে তাহাকে তুমি প্রতিপালনের জন্য দাদা এবং বউদিদির হস্তে অর্পণ করিও। রত্নেশ্বরকে দিয়া আবার তাহাকে কাড়িয়া লইয়াছি। দাদার বিবাহ আমিই দিয়াছিলাম। অদ্যাপি তিনি নিঃসন্তান। দাদার মনে ক্ষোভ আছে। তুমি এই সন্তান তাঁহাকেই মানুষ করিতে দিও। তুমি সোফিকে লইয়া কলিকাতায় বাস করিও। রত্নেশ্বর বংশের অভিশাপ ব্যর্থ করিবে বলিয়াই বিশ্বাস করি। রায়বংশ ধনে-পুত্রে লক্ষ্মী লাভ করিয়া সংসারে প্রতিষ্ঠা লাভ করুক।
পরমারাধ্য প্রিয়তম স্বামিন্ দাসী শ্রীচরণে বিদায় লইতেছে।
ইতি
প্রণতা
ভবানী।”
এ-চিঠিখানা রায়বাড়ীতে ছিল না। এ-চিঠি পরে পেয়েছি আমি অন্নপূর্ণা দেবী—রত্নেশ্বর রায়ের সহোদরার কাছে। তাঁর জন্ম ১৮৬২ সালে, ১৯৩৭ সালেও তিনি বেঁচেছিলেন। তখন তাঁর বয়স পঁচাত্তর বছর। তাঁর সঙ্গে পরিচয় ছিল না—তাঁকে দেখিনি আমি। এবং রায়বংশের সঙ্গে তাঁর বিয়ের পর থেকে কোন সম্পর্ক ছিল না। তিনি রাখেননি।
সুলতা—তার মূল কারণ জমিদারি এবং সম্পত্তি।
বিয়ের পর তাঁর সন্তান হতেই, তাঁর শ্বশুরেরা বীরেশ্বর রায়ের যে অর্ধেক অংশ পোষ্যপুত্র রত্নেশ্বরকে দান করেছেন, তার উপর দাবী তুলেছিলেন। বলেছিলেন—কন্যা জন্মাবার পূর্বে বীরেশ্বর পোষ্যপুত্র নিয়েছিলেন তাঁর সন্তান নেই বলে। কিন্তু পরে সন্তান যখন হয়েছে, কন্যাও সন্তান, তার সন্তানেরাই বীরেশ্বরের বিত্তাধিকারী, সুতরাং এই পোষ্যপুত্র-গ্রহণ সিদ্ধ নয়, এবং সে-সময় বীরেশ্বর রায় পক্ষাঘাতে অসুস্থ ছিলেন। সে-রোগ তাঁর কখনোই সারেনি। তার প্রমাণ, ভবানী দেবীর মৃত্যুর দেড় বছর পর আবার তিনি পক্ষাঘাতে একেবারেই পঙ্গু এবং স্মৃতি ও বাক্শক্তি হারিয়েছিলেন; তার কিছুদিন পরই তাঁর মৃত্যু হয়। এই অবস্থায় সই-করা দান এবং পোষ্যপুত্র গ্রহণ অসিদ্ধ। তা নাকচ হতে বাধ্য।
তোমার বাবা ব্যারিস্টার, তুমি নিজেও আইন মোটামুটি জান। এসব তোমার বুঝতে অসুবিধা হবে না।
পরে বিমলাকান্তের মধ্যস্থতায় এ-মামলা মেটে। তিনি অন্নপূর্ণাকে ডেকে রত্নেশ্বরের সামনে ভবানী দেবী যে চিঠি বীরেশ্বর রায়কে কাশী থেকে লিখেছিলেন, তাঁর পালক-পিতা যে-চিঠি লিখেছিলেন, যে-চিঠি দুখানা নিয়ে এসেছিল ছেদী সিং, সেই চিঠি এবং তার সঙ্গে এই চিঠি দেখিয়ে অন্নপূর্ণাকে নিরস্ত করেছিলেন মামলা থেকে। এবং এই চিঠিখানা তিনি চেয়ে নিয়ে বলেছিলেন—ওই চিঠিখানা আমাকে দিতে হবে। আমি রাখব।
তার সঙ্গে রত্নেশ্বর বোনকে দিয়েছিলেন এক লক্ষ টাকা। আর বিমলাকান্ত দিয়েছিলেন তাঁর নিজের সবকিছু।
অন্নপূর্ণাকে তিনিই মানুষ করেছিলেন। তিনি বিবাহ দিয়েছিলেন।
এই কথাবার্তার সময়েই ঠাকুরদাস পাল সমস্ত কথা শুনেছিল। এবং এই কথার জোরেই সে রত্নেশ্বর রায়কে বলেছিল, তোমার বংশের সব কুলুজী আমি ফাঁস করে দেব। এবং তার জন্যেই—।
সুলতার বুঝতে বাকী রইল না যে সুরেশ্বর বলতে চাইছে—তার জন্যই রত্নেশ্বর রায় পিদ্রু গোয়ানকে ইশারা করেছিলেন এবং সেই ইশারার হুকুম শিরোধার্য করে পিদ্রু তাকে ঝগড়া করতে টেনে নিয়ে এসেছিল কাঁসাইয়ের গোয়ানপাড়ার ঘাটে। এবং মুহূর্তে তার লুকানো ছোরাখানা বের করে ঠাকুরদাস পালের পেটখানা ফাঁসিয়ে দিয়েছিল। ঠাকুরদাস পালের পেটের মধ্যে রায়বাড়ীর গুপ্তকথা যা লুকনো ছিল, যা হজম হবার নয়, তা তার চিরে দেওয়া পেট থেকে রক্তের স্রোতের সঙ্গে বেরিয়ে মাটির মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল।
সুরেশ্বর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সিগারেট ধরালে। তারপর বললে-এর পর বীরেশ্বর রায়ও একরকম মরা মানুষ। রত্নেশ্বর রায় তাঁর ডায়রীতে লিখেছেন—“একবার মাকে হারাইয়া ভ্রান্তির মধ্যে প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মায়ের মৃত্যুর পর আবার তিনি সেই প্রেতই হইলেন! আবার সেই মদ্যপান আরম্ভ করিয়াছেন। মাতাঠাকুরাণী নাকি সোফিয়াকেই তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতে এবং অহরহ তাঁহার কাছে থাকিতে অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন। মাতুলও তাহাই বলিলেন। বলিলেন—মাতৃদেবী এইরূপই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাঁহার নিকট। সোফিয়া বাঈ মুসলমানের কন্যা। পেশায় সে বাঈজী। বহুজন- ভজনাই তাহার জীবিকা। সেই সোফিয়া বাঈও পিতৃদেবের আচরণে ভীত হইয়া পড়িয়াছে। সে পাগলাবাবার কাছে দীক্ষা লইয়া এখন হিন্দুর আচরণেই থাকে। তাহার কর্মগুলি সে অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত পালন করে। কিন্তু পিতৃদেব (দেবতা বলিতে সঙ্কোচ হয়) হয় উন্মাদ, নয় জীবনকালেই প্রেতে পরিণত হইয়াছেন। তাঁহার নিকটে যাইতে ইচ্ছা হয় না, আমার ক্রোধ হয়, ঘৃণা হয়, লজ্জাও হয়। আমার দেবীতুল্যা মাতৃদেবীর নিন্দা এবং তাঁহাকে প্রকারান্তরে গালিগালাজই করিয়া থাকেন।
বলেন, আমার জীবন সে বিষময় করিয়া দিয়া গিয়াছে। সারাটা জীবন একটা সুন্দরী প্রস্তর নারী-মূর্তিকে আলিঙ্গন করিয়া আমার সারা দেহ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছে। তপস্বিনী-সতী-শাপভ্রষ্টা দেবীকে বিবাহ করিয়া আজ আমার এই অবস্থা। আমি ভালবাসিলাম তাহাকে, সে আত্মসমর্পণ করিল দেবতাকে। আমাকে সারাজীবন ক্ষত-বিক্ষত করিয়া, জীবনের একটা কণা না দিয়া আমার হৃদয়ের ক্ষোভের তুষের স্তূপে আগুন জ্বালাইয়া দিয়া দেবলোকে চলিয়া গেল। আমি তুষানলে দগ্ধ হইতেছি, নিষ্ঠুর যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। ইহাই সতীত্বের এবং নারীধর্মের উৎকৃষ্টতম আদর্শ।
সোফিয়া হউক বাঈজী, হউক সে সকলের চক্ষে ঘৃণিতা, পতিতা, হউক সে বিধর্মী তথাপি সে-ই আমার সান্ত্বনার উৎস, সে-ই আমার শান্তি, সে-ই আমার সব।
সমাজ ইহাতে আপত্তি করিলে আমি সমাজ ছাড়িব। আত্মীয়স্বজন এমন কি তুমি পুত্র, তুমি আপত্তি করিলে তোমাকেও পরিত্যাগ করিব। আমাকে বলিলেন—তোমার ঘৃণা হয় তুমি আসিয়ো না। ইচ্ছা না হইলে বা লজ্জা বোধ করিলে আমার মুখাগ্নি বা শ্রাদ্ধ করিয়ো না। স্বর্গে, মুক্তিতে আমার লোভ নাই, কামনা নাই এবং তোমার মত দেবোত্তরভোগীও আমি নহি যে আমাকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে।
আমার কলিকাতার সম্পত্তি আছে। ইহা দেবোত্তরের অন্তর্গত নহে, ইহার পত্তন করিয়াছিলেন কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্য। তিনি প্রথম যৌবনে মুসলমানীকে বৈষ্ণবী করিয়া ঘর বাঁধিয়াছিলেন, কাহাকেও গ্রাহ্য করেন নাই; আমার পিতা একটা অজাতের মেয়েকে লইয়া তাহাকে যোগিনী বলিয়া জাহির করিয়া প্রকাশ্যে কীর্তিহাটে রাখিয়াছিলেন। আমি সোফিয়াকে লইয়াই জীবনযাপন করিব, আমি যদৃচ্ছা জীবনযাপন করিব। ইহাতে কাহারও কোন কথা শুনিব না। মদ্য আমি পান করিব। চিকিৎসকের কথাও আমি মানিব না। তাহাতে আমার যাহা হয় হইবে। চিকিৎসকেরা বলিয়াছেন—আবার আমি পঙ্গু হইতে পারি। হইলে যতক্ষণ অর্থ আছে, ততক্ষণ আমার সেবার কোনরূপ অভাব হইবে না। তুমি পুত্র হইয়া আমাকে সদুপদেশ দিতে আসিয়ো না।
তুমি তোমার শ্বশুরের পরামর্শে—তিনি ডেপুটি সাহেব, হাকিম লোক, তাঁহার পরামর্শ আইনানুসারে ভাল, তুমি জমিদারী আইন অনুসারে চালনা করিতেছ; বলিতেছ এ-যুগ নতুন যুগ। উত্তম কথা। তাহাই চল। বলিতেছ—এ-যুগে যাহারা ভদ্র, যাহারা শিক্ষিত, যাহারা অভিজাত, তাহারা আর আগের নিয়মে চলে না। তুমি তাহাই চল।
আমার কাছে আমাকে এরূপ ভাবে উত্ত্যক্ত করিতে আসিয়ো না। তাহার শ্রাদ্ধে আমি যাইব না। তাহাতে তোমার মাথা হেঁট হইবে, তুমি ফিরিয়া যাও।
রত্নেশ্বর রায়ের দারুণ ক্রোধ হয়েছিল। তিনি বীরেশ্বর রায়ের চেয়ে কম ক্রোধী ছিলেন না। তবু তিনি ছিলেন সংযমী এবং ছেলেবেলা থেকে জীবনের শিক্ষাও ছিল অন্যরকম। তাছাড়া জমিদারীতে আপন অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আর একজন অভিভাবকের অধীন হয়েছিলেন—যিনি ছিলেন ব্রাহ্মভাবাপন্ন লোক, তারপর পেশায় ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। এবং রত্নেশ্বর রায় তাঁর ডায়রীতে বীরেশ্বর রায় সম্পর্কে মিলনের পর যতই আবেগ এবং শ্রদ্ধা প্ৰকাশ করে থাকুন, তাঁর বাল্যকালে বীরেশ্বর রায় সম্পর্কে যে বিরূপ মনোভাব পোষণ করেছিলেন, সেটা সাময়িকভাবে চাপা পড়েছিল মাত্র। মায়ের জীবিতকালে সে মুখবন্ধ গর্তের সাপের মত চাপা ছিল; মায়ের মৃত্যুর পর সুযোগ পাবামাত্র তার বিষ নিঃশ্বাসে আর মুখে করে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল।
তিনি বাপকে মায়ের শ্রাদ্ধে বলতে এসেছিলেন। ভবানী দেবীর মুখাগ্নি করেছিলেন বীরেশ্বর রায়। রত্নেশ্বর তখন কীর্তিহাটে। এবং তখন সরস্বতী-বউ স্বর্ণলতা চার-পাঁচ মাস অন্তঃসত্ত্বা। এবং সন্তান প্রসব করে তিনি মারা যাবেন এ-কথা কেউ ভাবেওনি। চিকিৎসকেরাও না। প্রসবের তিন-চার দিন পর মারা গেলেন ভবানী দেবী, সুতরাং মৃত্যু আকস্মিক। রত্নেশ্বরের অনুপস্থিতিতে বীরেশ্বর শেষকৃত্য করেছিলেন। দশদিনে অশৌচান্তের সময় রত্নেশ্বর এসে পৌঁছেছেন; একলাই পৌঁচেছেন; সরস্বতী-বউয়ের বাপ এস-ডি-ও সাহেব ডাক্তারদের পরামর্শমত কন্যাকে তখনকার দিনে ট্রেনে যেতে দেননি। রত্নেশ্বর একলা গিয়েছিলেন। পরে এক বছর পরে প্রথম বার্ষিক শ্রাদ্ধের সময় রত্নেশ্বর কীর্তিহাটে চন্দনধেনুসহ দানসাগর ক্রিয়া করে সমারোহ করেছিলেন, সেই শ্রাদ্ধের সময় বাপকে বলতে এসেছিলেন যাবার জন্য। বীরেশ্বর রায় বলেছিলেন—না। তখন তিনি আবার মদ ধরেছেন। এবং এ সম্পর্কে পিতা-পুত্রে কিছু পত্রালাপ হয়েছে। সেদিন বিস্ফোরণ হয়ে গেল। এবং সেই দিনই বীরেশ্বর রায়ের আবার নূতন করে পুরানো ব্যাধি দেখা দিল। শরীর অসুস্থ হল।
এর ছ’মাস পর তিনি মারা গেলেন। তাঁর শয্যার পাশে সোফিয়া আর মহেন্দ্র ছাড়া আর কেউ ছিল না। অবশ্য নীচে এবং বাড়িতে লোকজন কলকাতার ম্যানেজার থেকে দারোয়ান-টারোয়ান সবই ছিল।
রত্নেশ্বর এসেছিলেন। কিন্তু তিনি এসে উঠেছিলেন তাঁর শ্বশুরের বাড়িতে জোড়াসাঁকোয়- তার কারণ তিনি এসেছিলেন সস্ত্রীক। স্বর্ণলতার কোলে তখন প্রথম সন্তান। সোফিয়াকে নিয়ে যে বাড়ীতে বীরেশ্বর রায় বাস করেন, সে-বাড়ীতে তিনি এসে ওঠেননি। সেই সময় থেকেই এ বাড়ীতে ওঠা বন্ধ করেছিলেন। রাত্রি একপ্রহর পর্যন্ত থেকে তিনি ফিরে গিয়েছিলেন শ্বশুরের বাড়ীতে। তখন অবশ্য অবস্থা এমন খারাপ ছিল না। ডাক্তার একজন বাড়ীতে মোতায়েন ছিল। হঠাৎ মধ্যরাত্রে অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে তিনি অজ্ঞান হয়ে যান এবং কয়েক ঘণ্টা পরই মারা যান।
অবস্থা খারাপ হতেই রাত্রে গাড়ী গিয়েছিল। কিন্তু ১৮৬৩ সালের কলকাতা। পথঘাট একালের মত পিচঢালা পথ নয়। এবং জানবাজার থেকে জোড়াসাঁকো পর্যন্ত বড় রাস্তা মাত্র একটি। চীৎপুর রোড। আর একটা কলেজ স্ট্রীট-কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কিন্তু সেদিক থেকে জোড়াসাঁকো যেতে অনেক আঁকা-বাঁকা অপরিসর রাস্তা এবং সংকীর্ণ গলি। দুপাশে টিমটিমে কেরোসিনের আলো। তাও দুরে দুরে। সুতরাং পৌঁছুতে দেরী হয়েছিল এবং ডাকাডাকি করে রত্নেশ্বর রায়কে তুলতেও সময় লেগেছিল। তারপরও দেরী হয়েছিল তাঁর বের হতে।
সুলতা, রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীতে এসব কথা আছে। কিন্তু ঠিক এভাবে নেই। তিনি সত্যবাদী ছিলেন, মিথ্যা কথা ডায়রীতে লেখেন নি। কিন্তু অন্যত্র যেভাবে তিনি তাঁর মনকে প্রকাশ করেছেন, তা এই ঘটনার ক্ষেত্রে নেই।
শুধু লিখেছেন-”উঠিয়াও একটা কারণে বাহির হইতে বিলম্ব হইল। স্বর্ণলতাকে এই রাত্রে লইয়া যাওয়া ঠিক হইবে কিনা স্থির করিতে বিলম্ব হইল। অবশেষে এই শীতের রাত্রে ছোট ছেলে লইয়া যাওয়া ঠিক উচিত বোধ হইল না, অতএব আমি একাই বাহির হইলাম, বাহির হইবার সময় অঞ্জনা বলিল-আমি যাই। কারণ এ সময় অনেক সাংসারিক মঙ্গলের কাজ থাকে। ও-বাড়ীতে তো একা সেই বাঈ ছাড়া মেয়েছেলে কেউ নাই! সে সব আমিই করিব। ইহা খুবই সমীচীন মনে হইল। অগত্যা তাহাকে সঙ্গে লইয়াই সেই শীতের শেষ রাত্রে রওনা হইয়া যখন জানবাজার আসিয়া পৌঁছিলাম তখন আমার পিতা দুর্দান্ত দুর্ধর্ষ বীরেশ্বর রায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। বড়ই দুঃখ বোধ করিলাম। অনুশোচনাও হইল। গত রাত্রে এখানে থাকিলেই হইত। না হয় ফলটল খাইয়াই থাকিতাম। হায় এমন দুর্দান্ত, দুর্ধর্ষ পুরুষ, বিশালকায় বীরপুরুষ আজ চিরনিস্তব্ধ। আমার নয়ন-যুগল হইতে অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। বক্ষের মধ্যে একটা বেদনা অনুভব করিলাম। সেই সমারোহময় পুরুষ আজ নিঃসঙ্গ অবস্থার মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। অথবা ইহাই তাঁহার উপযুক্ত হইয়াছে। তিনি সংসারে একা থাকতে চাহিয়াছেন, সাধ্বী স্ত্রীর প্রতি বিরাগের অন্ত ছিল না, আমি পুত্র আমার সহিত আজ এক বৎসর পত্র ভিন্ন সাক্ষাৎ করেন নাই। আজীবন এক বাঈজীকে লইয়াই জীবনাতিপাত করিলেন। ঈশ্বর মানিতেন না। কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না। সুতরাং এ-প্রকার মৃত্যুই তাঁহার উপযুক্ত এবং বিধাতা কর্তৃক অবধারিত ছিল।”
সুরেশ্বর একটু চুপ করলে। সুলতা বললে-রত্নেশ্বর রায় একজন অসাধারণ মানুষ ছিলেন সুরেশ্বর। একটা সত্যকারের ক্যারেক্টার। অত্যন্ত শক্ত মানুষ!
সুরেশ্বর বললে—হ্যাঁ, তা ছিলেন। সে-কথা আমি আমার জবানবন্দীর মধ্যে বার বার বলেছি। সেই কারণেই যে দুটো হত্যা তিনি করিয়েছিলেন, তার অপরাধ বিবেচনা করতে গিয়ে সম্ভ্রমভরে পিছিয়ে এসেছি। মনে মনে বলছি, তোমার বিচার অন্য যারা শুনবে, জানবে, তারা যা বলে বলুক, যা করে করুক, আমি শুধু তোমার কাজের জবানবন্দী দিয়েই খালাস।
তবে এক্ষেত্রে, তাঁর ডায়রী থেকে যা পেয়েছি, তার বাইরেও আরো কিছু আছে। সেটা জেনেছিলাম আমি রত্নেশ্বর রায়ের সহোদরা অন্নপূর্ণা দেবীর কাছে। এক্ষুনি আমি তোমাকে বললাম- ভবানী দেবীর এই পত্রখানা পেয়েছি আমি তাঁরই কাছে। ১৯৩৭ সালেও পঁচাত্তর বছর বয়সে তিনি বেঁচেছিলেন।
১৮৬৩ সাল থেকে কিছুক্ষণের জন্য ১৯৩৭ সালে এস সুলতা।
১৯৩৭ সালে যে সময় গোপাল সিংয়ের প্রপৌত্র শিবু সিং নামক ভাল ছেলেটি বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েও তার বাপের কাছে রায়বাড়ীর অত্যাচারে তার দুর্ধর্ষ এবং প্রবল প্রতাপ প্রপিতামহ গোপাল সিংয়ের সর্বনাশের এবং চরম অপমানের গল্প শুনে বিপ্লবীর ধর্ম বিসর্জন দিয়ে, দেশের স্বাধীনতার মূল্যবোধ জলাঞ্জলি দিয়ে, সরকারী সাক্ষী হয়ে বীরেশ্বর রায়ের প্রপৌত্র, রত্নেশ্বর রায়ের পৌত্র, শক্তিহীন দেউলে জমিদার শিবেশ্বর রায়ের পুত্র—তাদের অঞ্চলের বিপ্লবী গোষ্ঠীর নায়ক অতুলেশ্বর কাকার বিরুদ্ধে এজাহার দিলে এবং নির্দোষ আমার মেজদিদিকে সুদ্ধ ধরিয়ে দিলে, সেই সময় এল।
নিশ্চয় মনে আছে তোমার সুলতা যে, মেজদি আমাদের অর্চনাকে বাঁচাতে তাঁর কাছে গচ্ছিত রিভলবারটা নিজে নিয়ে বের করে দিয়ে এই শাস্তিটা নিজে নিয়েছেন। অৰ্চনা তাতেও নিজেকে সংযত করতে পারে নি; শান্ত নিরীহ বৈষ্ণব প্রকৃতির বিষয়ে অনাসক্ত মানুষ বিমলেশ্বর কাকাকে সুকৌশলে উত্তেজিত করে রায়বংশের রক্তের প্রষুপ্ত প্রচণ্ড ক্রোধকে জাগিয়ে তুলেছিল।
অর্চনা যে কথাটা বিমলেশ্বর কাকাকে বলেছিল, সেকথা তার মুখ থেকে বেরিয়েছিল যে অমোঘ শক্তিতে তা আমি শুনি নি, আমি শুনেছিলাম, বিমলেশ্বর কাকার স্ত্রীর মুখ থেকে, তাতেই আমার বুকেও আগুন জ্বলেছিল। বিমলেশ্বর কাকা বুকের জ্বালায় শিবুকে মারতে গিয়ে ধরা পড়লেন। আমি সেদিন রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রী পড়ে যাচ্ছিলাম। সকালের পর ও-বাড়ী থেকে যখন বিমলেশ্বর কাকাকে ধরে নিয়ে গেল কোমরে দড়ি বেঁধে তখন থেকেই পড়তে বসেছিলাম, খাইনি, স্নান করিনি, হুইস্কি স্পর্শ করিনি, খেয়েছিলাম কয়েক কাপ চা। রাত্রি হয়ে গিয়েছিল দশটা। শীতের দিন, কীর্তিহাট গ্রামে রাত্রি দশটা কম নয়। শেয়াল ডেকে গেছে, বিবিমহলের পাশে কাঁসাইয়ের ধারে জঙ্গলে পেঁচা ডাকছে। পেঁচার ডাক বড় কর্কশ সুলতা। কলকাতায় মানুষ তুমি, নিস্তব্ধ রাত্রে পেঁচার ডাক সম্ভবত তুমি শোন নি। বিবিমহল খুব বড় নয়, কিন্তু ছোটও নয়, বাড়ীটার মধ্যে আমি আর রঘু চাকর। রঘুও কিছুকাল কীর্তিহাটে বাস করে আর রায়বাড়ীর মহলগুলোয় ঘুরে রায়বাড়ীর মেজাজ খানিকটা পেয়েছিল। বিমলেশ্বর কাকার অপমানে সেও সেদিন দুঃখ পেয়েছিল। সেও আমাকে সেদিন খাবার কথা বিশেষ বলে নি। নিজেও খায় নি।
আমি ডায়রী পড়ছিলাম, হঠাৎ চৌদ্দ বাতির টেবিলল্যাম্পটা দপ করে নিভে গেল। সম্ভবত সন্ধেবেলা থেকে জ্বলতে জ্বলতে গরম হয়ে গ্যাস হয়েছিল। রঘুকে আলো জ্বালাবার জন্যে ডাকতে গিয়েও ডাকলাম না। একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে বসে রইলাম। ভাবছিলাম রায়বংশের কথা। রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীতেই পড়েছি, ভবানী দেবীর মৃত্যুর কথা। রত্নেশ্বর রায়ের সঙ্গে বীরেশ্বর রায়ের ওই তিক্ত কঠিন কথাগুলির কথা। তখনো আমি ভবানী দেবীর ওই চিঠির কথা ঘুণাক্ষরেও জানি না।
কি জানি কেন রত্নেশ্বর রায়ের কঠোরতা আমার এক্ষেত্রে ভাল লাগে নি। তাঁর ডায়রীর শেষ যে লাইনটা পড়েছিলাম, সেটা আমার মনে গাঁথা হয়ে আছে। তিনি লিখেছিলেন—সংসারে ন্যায় এবং নীতিই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। ন্যায়কে মাথায় করিলে স্ত্রী-পুত্র, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন সকলেই তার অপেক্ষা ক্ষুদ্র। ন্যায়ের জন্য প্রয়োজনে পিতা পুত্রকে পরিত্যাগ করেন, এমন দৃষ্টান্ত লক্ষ লক্ষ রহিয়াছে। স্ত্রীর অন্যায়ে স্ত্রীকে ত্যাগ এদেশে সাধারণ ঘটনা। পিতাকে লোকে পরিত্যাগ সচরাচর করে না, তাহার কারণ বিষয় শতকরা নিরানব্বুই ক্ষেত্রে পৈতৃক হইয়া থাকে। কিন্তু এদেশে রামমোহন রায়ের মত দৃঢ়চেতা পুরুষ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তিনি পিতাকে ত্যাগ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার আদর্শের জন্য পিতৃশ্রাদ্ধে বিগ্রহ ও শালগ্রাম শিলাকে ঈশ্বর বলিয়া মানিতে অসম্মত হইয়া মাতার সহিত বিরোধ করিয়া উঠিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন। আমার পিতা চিরদিনই স্বেচ্ছাচারী, কোন ন্যায়, কোন ধর্মকে মান্য করেন না। তিনি বাঈজীকে আমার দেবীতুল্য মাতৃদেবী অপেক্ষা উচ্চে স্থান দেন। আমার মাতাকে অভিশাপ দেন। তাঁহার প্রতি চিরদিনই আমার বিরাগ। মধ্যে বৎসর তিনেকের জন্য মাতার জন্যই তাঁহার অনাচার সহ্য করিয়াছি। কিন্তু মাতৃদেবীর অন্তে তাঁহার প্রতি পূর্ব বিরাগ আরো বৃদ্ধি পাইয়াছে। রায়বংশে তিনি অনাচার, ব্যভিচার এবং স্বেচ্ছাচারে অত্যাচারে সর্বাপেক্ষা কলঙ্কিত পুরুষ। সর্বাপেক্ষা দুর্দান্ত। তিনি আজ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। দুঃখ আমার হইতেছে। কিন্তু দুঃখ হওয়া বোধহয় উচিত ছিল না। আমাকেই তাঁহার মুখাগ্নি করিতে হইল। মনে মনে বলিলাম, আমি কামনা করি ‘তুমি মুক্তি লাভ কর,’ কিন্তু আমি জানি তোমার কর্মফলে তোমাকে বহু জন্মান্তর এই সকল কর্মের ফল ভোগ করিতে হইবে।’
অন্ধকারে বেদনাহত মন নিয়েই বসে ছিলাম।
রঘু বাইরের ঘরে বসেছিল, সে ঘরের অন্ধকার দেখে ঘরে এসে ঢুকল, আমি বুঝতে পেরে বললাম -থাক, আলো জ্বালতে হবে না!
ঠিক এই সময় নিচে থেকে ডাক শুনলাম, সুরেশ্বর! শুয়েছ নাকি?
কণ্ঠস্বর চিনতে পারলাম না। হেঁকে বললাম- কে?
—আমি জগদীশ্বর কাকা।
জগদীশ্বর কাকা? অর্চনার বাবা! খবর পেয়েছি সন্ধ্যার পর ফিরেছেন। এত রাত্রে আমার কাছে এসেছেন জগদীশ্বর কাকা কিসের জন্য। এসে সমস্ত খবর শুনে আর একটা সর্বনাশ বা ভয়ঙ্কর কিছু করে ফেলেছেন নাকি?
আমি তাড়াতাড়ি রঘুকে আলোটা জ্বালতে এবং ডায়রীগুলো সামলে রাখতে বলে বাইরে রঘুর ঘরে যে হ্যারিকেনটা জ্বলছিল, সেটা নিয়ে নেমে গেলাম। দেখলাম, জগদীশ্বর কাকা অর্চনার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছেন।
বুঝলাম একটা কিছু ঘটেছে। বললাম—এত রাত্রে জগদীশ্বর কাকা?
জগদীশ্বর কাকা বললেন—ওপরে চল বলছি। এসেছি এই সর্বনাশী হারামজাদীর জন্যে।
কোন প্রশ্ন করলাম না সেখানে। কারণ আমার সন্দেহ ছিল, কোন-না-কোন পুলিশের চর কোথাও ঘাপটি মেরে আছে। বিমলেশ্বর কাকাকে হাতকড়া দিয়ে, কোমরে দড়া বেঁধে গ্রাম ঘুরিয়ে তাদের কাজ তারা শেষ করেছে, এ কথা অন্তত আমার বিশ্বাস হয় নি।
উপরের ঘরে এসেই জগদীশ্বর কাকা অর্চনাকে ছেড়ে দিলেন এবং কঠোর কন্ঠে বললেন—চুপ করে দাঁড়া হারামজাদী। চুপ করে!
তারপর আমাকে বললেন—তুমি তো শুনেছ সব!
জগদীশ্বর কাকার শরীর থেকে গাঁজার গন্ধ বের হচ্ছিল।
আমি বুঝলাম কি বলছেন তিনি, বললাম—সবই তো আমার চোখের সামনে ঘটেছে। আমি তো ছিলাম।
—ন্যাকা সেজো না হে। বিমলের স্ত্রী, বর্ধমানের বউমা তোমাকে সব বলে নি? হারামজাদী পোড়ারমুখী যা সব বলত বিমলকে, সেসব কথা পুলিশের কাছে বলতে তুমি তাকে বারণ কর নি?
স্বীকার করলাম। বললাম—হ্যাঁ, বলেছিলাম। না হলে যে আজ ওকেও ধরে নিয়ে যেত জগদীশ্বর কাকা!
—যেতো, আপদ যেতো! আমি বাঁচতাম।
—এসব আপনি কি বলছেন জগদীশ কাকা!
হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন তিনি।—বলছি সাধে! তুমি জান, আমার শালার শালা পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টর, তার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ করে এসেছি, তারা আসবে, কথা পাকা হবে। দিনও ঠিক করে এসেছি : এই মাঘ মাসে। এখন হবে কি? করব কি? বলতে পারো?
হঠাৎ কান্না থামিয়ে প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়লেন, বললেন—আর হারামজাদী আমাকে মুখের ওপর বলে কি জান? ওর এতবড় আস্পর্ধা, এতবড় বুকের পাটা, ঘাড়ের ওপর তিনটে মাথা—বলে ওখানে আমি বিয়ে করব না। জোর করলে আমি বলব—আমি এ-সবের ভেতরে আছি। নয়তো আমি বিষ খাব। নয় গলায় দড়ি দেব।
এসব কথা আমি জানতাম। অর্চনা সেদিন আমায় বলেছিল। আমি বললাম—একটা কথা বলব কাকা?
মুখভঙ্গি করে আমাকে বললেন—তুমি বিয়ের ভার নেবে তো! যা খরচ করতে হয় তুমি
করবে! সে কথা ও আমাকে বলেছে।
আমি বললাম—হ্যাঁ, সে কথা আমি বলেছি ওকে। আমি কালই যেতাম আপনার কাছে কথাটা বলবার জন্যে।
জগদীশ কাকা আবার বদলালেন। এবার সংযত অথচ শাসনের সুরে বললেন—হ্যাঁ। তাই আমি জানতে এসেছি। ও আমাকে বললে। বললে, আমার বিয়ের কথা নিয়ে তোমরা ভেবো না। সুরেশ্বরদা বলেছে আমাকে, সে পাত্র ঠিক করে বিয়ে দেবে। যা খরচ হয় সে করবে।
—হ্যাঁ। তা করব আমি। আমি সে কথা আপনার সামনেই বলছি।
—না। সামনে বললে হবে না। আমার পায়ে হাত দিয়ে বল। আমি গাঁজা খাই, মদ খাই, যাই হই আমি তোমার কাকা, গুরুজন, আমার পায়ে হাত দিয়ে বল। আর তিন সত্যি কর।
তাই বললাম। এবং পায়ে হাত দিয়েও শপথ করলাম। তখন আবার বললেন —শুধু ও বললে হবে না। স্বজাতে স্বঘরে মানে পালটি ঘরে বিয়ে দিতে হবে। তুমি আধা বেহ্ম, আমি জানি। তুমি যে লেখাপড়া জানা যার-তার ঘরের ছেলে এনে বলবে এর চেয়ে ভাল পাত্র আর হয় না, সে হবে না।
সুরেশ্বর বললে—তোমাকে কি বলব সুলতা, আমি এই অধঃপতিত রায়বংশের সন্তানটির কথায় রাগ করতেও পারিনি, ঘৃণা করতেও সঙ্কোচ হয়েছিল, ইচ্ছে হয়েছিল কাঁদি। এক কোণে অর্চনা চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম। সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু চোখ দুটো হয়ে উঠেছে যেন জ্বলন্ত অঙ্গার। ধুক ধুক করে জ্বলছে। সে যেন এখনি ক্রোধে, ক্ষোভে ফেটে পড়বে বলে মনে হল।
আমি তৎক্ষণাৎ সেই প্রতিশ্রুতি দিলাম। বললাম—তাই হবে!
জগদীশ্বর কাকা বললেন—শোন, এই রায়বংশ সিদ্ধপুরুষের বংশ। অর্চনাকে সবাই বলে ও হল সতীবউরাণী। এই বংশে ফিরে এসে জন্মেছেন। বউরাণীর বাবা কালীসিদ্ধ মহাসাধক ছিলেন। ওকে সৎপাত্রে না দিলে সর্বনাশ হবে তোমার।
অর্চনা এবার সত্যই ফেটে পড়ল। চীৎকার করে উঠল, বাবা!
জগদীশ্বর রায় দুরন্ত ক্রোধী; গাঁজা মদ খেয়ে প্রায় বিকৃতমস্তিষ্ক। তাঁর বাপ, আমার ঠাকুরদা শিবেশ্বরের সমৃদ্ধি এবং জবরদস্তির আমলে তিনি জন্মেছেন, বড় হয়েছেন, ছেলেবেলা থেকে দুরন্ত, দুর্দান্ত। এক পুলিশ আর গভর্নমেন্ট ছাড়া কাউকে গ্রাহ্য করেন না। সেই তিনি পর্যন্ত চমকে উঠলেন তার সে চীৎকারে।
তার দিকে তাকিয়ে তাকে তিনি ধমক দিতে পারলেন না, সভয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।
অর্চনা বললে—তুমি এবার থামবে কিনা বল?
অপ্রতিভের মত জগদীশ্বর কাকা বললেন—থামব?
—হ্যাঁ থামবে। এবার তুমি যা বলবে আমি জানি। বিয়েতে যে টাকা সুরেশ্বরদা খরচ করবে, সেই টাকাটা তুমি নিজে চাইবে। বলবে তার থেকে সুরেশ্বর, টাকাটা তুমি দাও, আমি দেখে শুনে ভাল পাত্রেই ওর বিয়ে দিই। আমি জানি! তা হবে না। তুমি বাড়ী চল!
আমি বললাম—অৰ্চনা, চুপ কর। এসব কথা বলতে নেই। উনিই বা তা বলবেন কেন?
অৰ্চনা বলে উঠল—বলবেন। বলবেন। বলবেন! আমি জানি!
জগদীশ্বর কাকা মাথা হেঁট করে রইলেন।
অকস্মাৎ কোন চোরের লুকানো চোরাইমাল বেরিয়ে পড়লে যেমন তার মুখের চেহারা হয়, ঠিক তাই হয়ে গেল।
অর্চনা বললে—রঘু, তুই আমাকে আলো নিয়ে বড় জ্যেঠাইমার কাছে দিয়ে আয়।
বড় জ্যেঠাইমা—শিবেশ্বরের বড় ছেলে—ধনেশ্বর কাকার স্ত্রী।
খুড়ীমা বিচিত্র মানুষ। আজও পর্যন্ত তার সঙ্গে আমার কদাচিৎ দেখা হয়েছে। তাঁর বড় ছেলে বিচিত্র চরিত্র মধুরভাষী আমার ব্রজদা, ব্রজেশ্বর। এবং তার সেজ ছেলে সেই দানবটি, যে সুখেশ্বর কাকাকে হত্যা করেছিল।
লোকে বলে এই দুই প্রকৃতিই তাঁর মধ্যে আছে। খুব বড় ঘরের কন্যা। পড়েছিলেনও ভাল ঘরে। ব্রজদার মত মিষ্ট কথা। আবার রাগলে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। কিন্তু একটা বড় গুণ আছে, কেউ আশ্রয় চাইলে সেখানে তিনি আশ্চর্য মানুষ। তাঁর নিজের সন্তানের চেয়েও বড় মমতায় তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে থাকেন। জগদীশ্বর কাকা বড় ভাই ধনেশ্বরকেও ভয় করেন না। কিন্তু বড় বউঠাকরুণ “কি হচ্ছে ঠাকুরপো”! বলে বের হলে, আর তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় না। সাড়া পেলেই সরে পড়েন!
কথাটা বলেই হনহন করে চলে গেল অৰ্চনা।
***