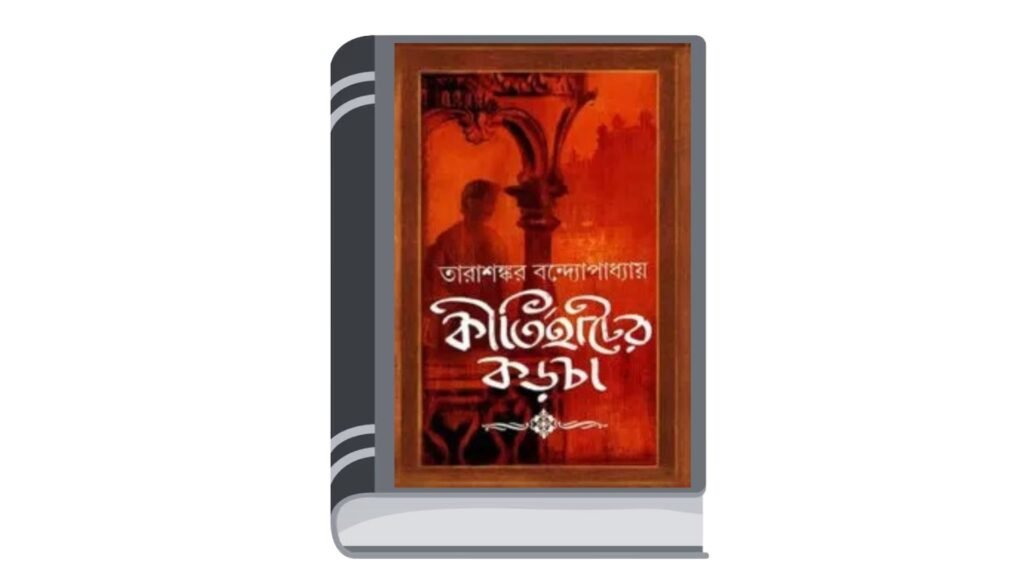কীর্তিহাটের কড়চা – ৪র্থ খণ্ড – ৫
৫
কলকাতায় দেবেশ্বর রায় কীর্তিহাটের রাজাবাবুর যুবরাজ। বাইরে শান্ত প্রসন্ন কিন্তু জীবনে ক্ষুরের মত ধার, শাণিত তরবারির মত আস্ফালন এবং শক্তি, তিনি সহ্য করবেন কেন?
তিনি একদিন গোপালদাসকে ডেকে বললেন-গোপালদা, তুই হয় ভায়লেটকে এনে দে, নয় বিষ এনে দে। গোপালদা, আমি বিষ খেয়ে মরব। আমি ভায়লেটকে ছাড়া থাকতে পারছি না। পারব না।
গোপালদা সঙ্গে সঙ্গেই সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল-তার জন্যে কি হয়েছে, দেবু আমার রাজাভাই। এনে আমি তাকে এখুনি দিতে পারি। কাল বল কাল যাব, তিন দিন—তিন দিনের মধ্যে ভায়লা-বউরাণীকে এনে দেব। সে নিশ্চয় আসবে। বলামাত্র আসবে আমি জানি। কিন্তু এখানে এনে রাখবে কোথায় বল? একটা বন্দোবস্ত কর আগে! এ-বাড়ীতে তো রাখা যাবে না, রাজাভাই। এখুনি খবর যাবে দপ্তর থেকে—এখানকার এই আমলা বেটারা বড় বজ্জাত। আমাকে সেদিন খাজাঞ্চী বললে—আমি দশটা টাকা চাইতে গিয়েছিলাম, তোমার রোকা নিয়ে, বললে—দেবুবাবুকে বলগে কিসের জন্য টাকা চাই লিখে দিতে হবে। আর তুমি এমন করে দেবুবাবুর সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা গায়ে গা লাগিয়ে ঘুরো না। কত্তা চিঠি দিয়ে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন।
ষোল বছরের জমিদার-পুত্র-বুদ্ধিতে, সাহসে অসাধারণ ছিলেন দেবেশ্বর। পরবর্তীকালে তার প্রমাণ তিনি প্রতি পদক্ষেপে রেখে গেছেন এবং যে সময়ের কথা বলছি, তার ক’মাস পরেই পিতাপুত্রে যে পত্র বিনিময় হয়েছিল, যে-পত্রের মধ্যে এই সমস্ত কথা তিনি খুলে লিখেছেন নির্ভয়ে, তাই তার প্রমাণ। তবুও প্রথমটা গোপালদার প্রশ্নটা দমিয়ে দিয়েছিল দেবেশ্বর রায়কে।
ভায়লেটকে, তাঁর ভায়লাকে এনে রাখবেন কোথায়? রাখতে হলে বাড়ী চাই, সুন্দর বাড়ী খাট চাই, পালঙ্ক চাই, আয়না চাই, আসবাব চাই; ভায়লার জন্য পোশাক চাই, পরিচ্ছদ চাই, তার কাছে কাজ করবার জন্য লোক চাই, জন চাই; তাকে সাজাবার জন্য অলঙ্কার চাই—অনেক কিছু চাই।
সামনে তখন তাঁর পরীক্ষা। এন্ট্রান্স পরীক্ষা। সেই দারুণ চাঞ্চল্যের মধ্যেই পরীক্ষা দিয়েছিলেন। পরীক্ষার পরই এই চিঠি তিনি লিখেছিলেন তাঁর বাল্যসঙ্গিনী পিসী অন্নপূর্ণা দেবীকে। তখন তিনি কাশীতে।
অন্নপূর্ণা দেবী সে চিঠি পেয়ে ভাইপোকে চিঠির উত্তর দেন নি; একটি লাল টুকটুকে কনে খুঁজতে শুরু করেছিলেন কাশী অঞ্চলেই। পাটনা, কাশী, এলাহাবাদ, আগ্রা অঞ্চলে তখন বাঙালীরা দলে দলে বাস করছেন এবং ওসব অঞ্চলে ওঁরাই হয়েছেন প্রধান এবং সরকারী অনুগ্রহে প্রবল। ডাক্তার বাঙালী, উকিল বাঙালী, ডেপুটি বাঙালী, সাব-ডেপুটি বাঙালী। বাঙালীরা তখন আই-সি-এস হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর সুরেন বাঁড়ুজ্জে, রমেশ দত্ত, বিহারীলাল গুপ্ত পাশ করে এসেছেন। বাঙালী তখন ভারতবর্ষে দিগ্বিজয় করছে ইংরিজী বিদ্যে আর ইংরেজের পৃষ্ঠপোষকতায়। তাদের অনেকজন প্রদেশান্তরে নতুন বটগাছের মত শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে। কাশীতেই কি বাঙালী তখন কম? কাশী আর বৃন্দাবন—এ-দুটি তীর্থই তো বাঙালীর তীর্থ। কাশীর ‘বাংগালী টোলাকে ভয় এবং খাতির কাশীধামের পাণ্ডারাও না করে পারত না। বৃন্দাবনে বাঙালীর খাতির আরও বেশী।
বিশেষ করে রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুরকে যে খাতির ইংরেজ সরকার দেখিয়েছিল, তা দেখে সারা ভারতবর্ষ চমকে গেছল। রাজা নবকৃষ্ণ ছিলেন ক্লাইভ সাহেবের দেওয়ান। তাঁর পোষ্যপুত্রের ছেলে রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুর-তিনি ইংরেজের অনুগত ছিলেন কিন্তু তাদের অযথা আনুগত্য দেখান নি। তাঁর ব্যক্তিত্বের এবং কীর্তির জন্যে ইংরেজ সরকার তাঁকে কে-সি-আই-ই খেতাব দিয়েছিল। তখন তিনি বৃন্দাবনবাসী। গৃহত্যাগ করে চলে এসেছেন বৃন্দাবন। খেতাব নিতে তিনি গেলেন না কলকাতা লাটসাহেবের দরবারে। লিখলেন—আমি হিন্দু, আমি বাণপ্রস্থ নিয়ে বৃন্দাবনে এসেছি; এখান থেকে আর আমার কলকাতা ফেরার উপায় নেই। তাতে আমাকে ধর্মভ্রষ্ট হতে হবে।
শেষ পর্যন্ত আগ্রায় স্পেশাল দরবার করে লাটসাহেব তাঁকে খেতাব দিয়েছিলেন। আগ্রা নাকি বৃন্দাবনের দ্বাদশবনের মধ্যে প্রথম বন—’অগ্রবন’। সেখান পর্যন্ত এসেছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুর।
* * *
—কোত্থেকে কোথায় যাচ্ছ, সুরেশ্বর। বাঙালীর সেকালের মহিমা আমার জানা আছে। তুমি তোমার দেবেশ্বর রায়ের কথা বল।
হেসে সুরেশ্বর বললে—জানা আছে তা জেনেও আমার সন্দেহ হয় সুলতা, জানাটা বেশ মনে মনে তলিয়ে বিচার করে জানা তো! আজকে যারাই স্বাধীন দেশে পলিটিক্যাল পার্টির মধ্যে আছে, তারা সবাই তোমরা প্রমাণ করতে ব্যস্ত যে, তোমাদের পূর্বপুরুষরা সে পলাশীর যুদ্ধের পর থেকেই ইংরেজের সঙ্গে শত্রুতা সেধে আসছে, কোন অনুগ্রহ নেয় নি বা নাও নি। বাড়ীতে কেউ লাঠিতে তেল মাখিয়ে, কেউ গাদা-বন্দুক নিয়ে ইংরেজ তাড়াবার কল্পনা করেছ। আমরা যারা জমিদার রাজা বা ধনীদের বংশধর, সব অপরাধ আমাদের।
অর্চনা হেসে বললে—সুরোদা, হঠাৎ তুমি যেন মেজাজের ব্যালান্স হারিয়েছে। বুঝেছি তুমি কেন সেটা হারিয়েছ।
চুপ করে গেল সুরেশ্বর। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সামনে তাকিয়ে রইল। কয়েক মুহূর্ত পরেই সুলতা সবিস্ময়ে দেখলে, সুরেশ্বরের বড় বড় চোখদুটি কানায় কানায় জলে ভরে উঠেছে। সুরেশ্বর চোখের পাতা বন্ধ করতে পারছে না, ভয় হচ্ছে, চোখের পাতার চাপে জল গড়িয়ে ঝরে পড়বে।
—সুরেশ্বর!
—আমি বলছি সুলতাদি। আমি বলি। রায়বাড়ীর এই জবানবন্দীর সবটাই আমি জানি। সুরোদা আর কাউকে বলে নি কিন্তু আমাকে না বলে পারে নি। আমি জানি।—
অর্চনা বললে—কথাগুলো যা তোমাদের হচ্ছিল, তা ওঘরে বসে আমি শুনছিলাম, আর কুড়ারাম রায়ের পাঁচালীর নকলখানা পড়ছিলাম। আমি ভাবছিলাম। ঠিক এই রকমই ভেবেছিলাম সুলতাদি। অবশ্য তুমি রাগ করবে এটা বুঝতে পারি নি। কারণ এখনও ঠিক যেন মনে ধারণাই করতে পারি না, তুমি কোন রকমে কীর্তিহাটের রায়েদের ভালমন্দ তারা যা করেছে তার সঙ্গে জড়ানো আছ। থাকার তো কথা নয়। রায়বাড়ীর কর্তাদের হাত যাদের উপর পড়েছে, তারা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ভেঙে গেছে। তবে কিছু কিছু লোক আছে, যারা সত্যিই খুব বড় হয়েছে। তারা অবশ্য রায়বংশের কাউকে এখন আমলে আনে না।
সুরোদার ঠিক এমন ধরনের কিছু হবে, মানে চঞ্চল হবে, কি ছেলেমানুষের মত কেঁদে-কেঁদে ফেলবে, আমি তা ভেবেছিলাম। এইভাবে যখন ও চঞ্চল হয় তখন খানিকটা পাগলের মত হয়ে যায়। বড়ঠাকুরদা দেবেশ্বর রায়কে ও বড্ড ভালবাসে। তাঁর ঋণ যেটা তার মধ্যে রায়বংশের পুরনো শ্যামাকান্তের ঋণকে আবিষ্কার করেছে। বলে, দেবেশ্বর রায় সে ঋণটা শোধ করতেন, করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা করতে তাঁকে দেননি; দেননি আমার দাদাশ্বশুরের মা, দেবেশ্বর রায়ের পিসীমা, সুরোদার অন্নপূর্ণা-মা, আমি তাঁকে বলতাম—বড়মা।
আমার বিয়ে হবার পর ওই নামেই তাঁকে ডাকতাম। আমার বিয়ে হল, এই জানবাজারের বাড়ী থেকেই বিয়ে হয়েছিল। বড়-জ্যাঠামশাই মানে যজ্ঞেশ্বর রায় আসেন নি, ছেলেরাও কেউ আসে নি, কিন্তু দুপুরবেলার দিকে ট্যাক্সি করে জ্যাঠাইমা এসেছিলেন। সঙ্গে একজন ঝি। একটা আংটি দিয়ে গিয়েছিলেন। এখান থেকে হরিশ মুখুজ্জে রোডের বাড়ীতে বড়মার সঙ্গেও দেখা করে প্রণাম করে গিছলেন। বিয়ের মাস দুয়েক পরই বড়মা, আমার অন্নপূর্ণা-মা অসুখে পড়লেন। যেন এই বিয়েটার অপেক্ষাতেই তিনি ছিলেন। বলতেনও, আমাকে বলতেন-দেখ, তুই গতজন্মে আমাকে জন্ম দিয়েই পালিয়েছিলি। দেখ, সংসারে প্রসব করে সন্তানের সেবা আর ঈশ্বরের সেবা দুই সমান। সে যে না করে তার জীবনে ঋণ থাকে, জন্মান্তরে শোধ করতে হয়। সেই শোধ করতে এসেছিস। নে, বেশ করে সেবা কর; তেল গরম করে এনে পায়ে মালিশ কর, পিঠে মালিশ কর। আমি আর ঝিয়ের কাজ নেব না।
দু মাস পর হঠাৎ জ্বর হল। ঘুসঘুসে জ্বর। আমার স্বামীই দেখছিলেন। বললেন—কিছু না। হেসে বড়মা বললেন—কিছু না নয় রে, তোর বউয়ের সঙ্গে আমার আর জন্মের মার সঙ্গে হিসেব-নিকেশের পালা পড়ল। খতেনের খাতা খুলে বসেছে হিসেব-নিকেশওয়ালা। সুদে আসলে এতদিনে সেবা আমার কত পাওনা হয়েছে।
আমার স্বামী এসবে বিশ্বাস করতেন না, সুলতাদি। তিনি নতুন কালের নতুন মানুষ মানে যেকালে আমার বিয়ে হল ১৯৩৭ সালে, সেকাল থেকেও অনেক পরের কালের মানুষ। এরা চালাক, এরা চতুর, এরা মুখে বলে এরা যুক্তিবাদী কিন্তু আসলে এরা অবিশ্বাসবাদী, মানে জীবনে কোন বিশ্বাস নেই। যা আজকাল, মানে মহাযুদ্ধের পরে, স্বাধীন ভারতবর্ষে সব মানুষের মধ্যে দেখতে পাচ্ছ। তিনি লুকিয়ে মদ খেতেন, তিনি…। চুপ করে গেল অর্চনা। কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসছিল।
কিছুক্ষণ চুপ করে সামলে নিয়ে সে বললে-এই এমন একটা বাড়ী যা বাইরে থেকে একেবারে আদর্শবাদের মন্দিরের মত মনে হত, সেই বাড়ীর কোণে কোণে এই কালের, এই ধারার তখন শুরু হয়ে গেছে।
যাক গে, যা বলছিলাম বলি। রায়বাড়ীর জবানবন্দী কীর্তিহাটের কড়চা যা সুরোদা ছবিতে এঁকেছে, তার মধ্যে দেবেশ্বর-ঠাকুরদার প্রথম জীবনের সব কথাই জমা ছিল, এই বড়মা, সুরোদার অন্নপূর্ণামা’র কাছে। তিনি নিজে নিজের মৃত্যুর কথা জানতে পেরেছিলেন, বুঝতে পেরেছিলেন। তাই দিন পনেরো পর চিঠি লিখে ডেকে পাঠালেন সুরোদাকে। আমাকে দিয়েই লেখালেন, এবার আমি যাইব। আমার কাজ শেষ হইয়াছে, আমার মায়ের আসন পাতিয়া দিয়াছি; এবার আমার ডাক আসিয়াছে। আমি যাইব। তোমাকে কিছু বলিবার আছে, তোমাদের বংশের কিছু কাগজপত্র আমার নিকট আছে। তাহা তোমাকে দিতে চাই এবং তোমাকে কিছু বলিতেও চাই।
সুরোদা চিঠি পেয়ে এল। বড়মা তার আগে তার সেই পুরনো মেহগনি কাঠের হাতবাক্সের মধ্য থেকে বান্ডিল বাঁধা চিঠির তাড়া খুলে বসে বেছে বেছে খান বারো-চৌদ্দ বের করলেন। বললেন—চিঠিতেই সব আছে; এতেই সব পাবি। কিন্তু ঠিক ধরতে পারবি নে। যেসব কথা সামনা-সামনি দেবুর সঙ্গে কি দাদার সঙ্গে হয়েছে, তা তো চিঠির মধ্যে নেই। তার থেকে আমি বলি, তুই শোন। সে অনেক কথা রে!
***
সেদিনের কথা আমার চোখের উপর ভাসছে সুলতাদি। কলকাতা পৌঁছেই সুরোদা এসে হাজির হন আমাদের বাড়ীতে। বড়মায়ের দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকলে—বড়মা!
বড়মা তার দিকে তাকিয়ে বললেন—এসেছিস! আয়। দেখ, ওই কথাগুলি বললেন। তারপর বললেন—আমার ডাক এসেছে। আমি এবার যাব। তাই কথাগুলো তোকে বলে যাচ্ছি, আর এই চিঠিগুলো সেই কথার দলিল, তোকে দিয়ে যাচ্ছি। তোকে মনে করিয়ে দিয়ে যাচ্ছি রে তোর দেনার কথা, তোর দায়ের কথা, তোর ইচ্ছের কথা।
সুরোদা বুঝতে পারলে না। অবাক হয়ে মুখপানে তাকিয়ে রইল, বড়মায়ের মুখের দিকে।
বড়মা বললেন—কি, কিছু মাথায় ঢুকছে না তোর?
সুরোদা হেসে বললে—না বড়মা, ঠিক ঢুকছে না! একটু গোলমাল ঠেকছে!
বড়মা বললেন—কই আমাকে রাঙাপিসী বলে ডাক তো! ওরে তুই যখন ছেলেবেলা বাপের সঙ্গে আসতিস, তখন আমার দেখলেই মনে হত, তুই আমার সেই দেবু। আমার গোরা ভাইপো! তাই তোকে ঠিক দেবুর ছেলেবেলার পোশাকের মত পোশাক তৈরী করিয়ে দিয়েছিলাম, তোর বাপকে বলেছিলাম—এই পোশাক পরিয়ে ওকে নিয়ে আসিস আমার কাছে। জ্বর হওয়া অবধি স্বপ্ন দেখছি, তুই এসে বলছিস-রাঙাপিসী, তোমার কাছে আমি যে সব দেনা করেছিলাম, তার হিসেবগুলো আছে, আমাকে বলে দাও। আমিই তোমার দেবু, রাঙাপিসী, গোরা ভাইপো। এই নামটি, গোরা নাম তাকে আমিই দিয়েছিলাম। গোরা মানে, সাহেব গোরা নয়, নবদ্বীপের গোরাচাঁদ।
জানালার ধার থেকে ফিরে এসে বসল সুরেশ্বর। বললে—তুই কথা বাড়িয়ে ফেলছিস অর্চনা। দে আমাকেই বলতে দে।
সুলতা, গোড়াতেই বলেছি এবং এখন অৰ্চনাও বলেছে, অন্নপূর্ণা-মা আমার চেহারার সঙ্গে আমার ঠাকুরদার মিল দেখতে পেতেন। শুধু অন্নপূর্ণা-মা কেন, মেজঠাকুরদা শিবেশ্বর রায়ও বলেছিলেন একথা। রায়বংশের শ্রেষ্ঠ সুপুরুষ ছিলেন আমার দাদা দেবেশ্বর রায়, তুমি তার মত, হয়তো তার থেকেও উজ্জ্বল। মিল যে আছে, সে তাঁর ছবির সঙ্গে মেলালে তুমিও বের করতে পারবে। তার উপর ঘটনাচক্রে জানবাজারের বাড়ীতে হঠাৎ কুইনি এবং হিলডাকে দেখে তাঁর পুরনো কথাগুলো, যেগুলো তিনি ভুলে যেতে বসেছিলেন, সেগুলো নতুন করে মনে পড়েছিল। শুধু মনে পড়া নয়, একটা ধাক্কা যা তিনি সেকালে খেয়েছিলেন, তা আবার নতুন করে তাঁর মনে পড়েছিল।
ঘটনাগুলো বলে যাই, তাহলেই তুমি বুঝতে পারবে, কেন তিনি কুইনিকে দেখে চঞ্চল হয়েছিলেন, কেন তিনি আমাকে বলেছিলেন, কুইনির বাড়ীখানা তাকে ফিরিয়ে দিতেই হবে তোকে। কেন তিনি বলেছিলেন—কুইনিকে লেখাপড়া শিখিয়ে জীবনের পথে দাঁড় করিয়ে দিতেই হবে তোকে। এবং কুইনিকেই বা তিনি কেন বলেছিলেন, সুরেশ্বরবাবু তোর পড়ার ব্যবস্থা করবেন। সেইমত পড়াশুনো করবি তুই, বুঝলি?
অবলীলাক্রমে বলেছিলেন। যেমন করে আপনার নাতি-নাতনী বা তাদের ছেলেমেয়েকে বলা যায় তেমনি করে বলেছিলেন। এমনটা তুমি কখনও অনুভব করেছ কিনা জানি নে, তবে আমি অনুভব করেছি। এই কুইনির সম্পর্কেই অনুভব করেছি। কিছুক্ষণ আগেই বলেছি, কুইনিকে নিয়ে ওর সৎমামা হ্যারিসের সঙ্গে ঝগড়ার যেদিন বিচার করতে গিয়েছিলাম, তার কদিন পর বিবিমহলে অর্চনার সঙ্গে কুইনি এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে এবং বাড়ীর দলিলটার সঙ্গে দেবেশ্বর রায়ের কখানা চিঠি সে আমাকে দেখতে দিয়েছিল। সে সব চিঠির মধ্যে আসল যা সত্য এবং জীবনের সঙ্গে জীবনের যে আসল সম্পর্ক তার একটা হিসেব ছিল। চিঠিগুলো পড়ে যখন মুখ তুললাম তখন কুইনি নেই। ওদিকে সূর্যাস্ত হচ্ছিল, সেই গোধূলির আলোয় শুকনো কাঁসাইয়ের বালুচর পার হয়ে কুইনি তখন শিলুটের ছবির মত চলে যাচ্ছিল।
সে ছবিটাও আমি এঁকেছি সুলতা। ছবিখানা আমার পরম প্রিয়। এই জবানবন্দীর মধ্যে সেখানার থাকা উচিত ছিল; কিন্তু নেই। ছবির বিচারে সেইখানাই আমার শ্রেষ্ঠ ছবি। আমার বিচারেই নয়, বিলেতের বিচারেও বটে। কিনতে চেয়েছিল অনেকে কিন্তু তা আমি দিই নি। ছবিখানা কুইনিই আমার কাছে চেয়ে নিয়েছিল।
এলিয়ট রোডের বাড়ীখানা কেড়ে নেওয়ার খবর পেয়ে যে কথা অন্নপূর্ণা-মা সেই জ্যাঠামশায়ের বাড়ী যাবার আগে আমাকে বলেছিলেন তা শুনেছ। সে চিঠিখানাও রয়েছে এখানে। পৃথিবীতে পুরুষ আর নারী নিয়ে দ্বন্দ্ব চিরকাল, সেই সৃষ্টির আদিকাল থেকে চলে আসছে। বিচিত্র ঘটনা এই যে, যে-কোন পুরুষ যে-কোন নারীকে পেয়ে খুশী নয়, সুখী নয়। সেকালে রাজা-রাজড়াদের ঘরে ধরে আনা এবং বিয়ে করা নারী তো কম থাকতো না; ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের পরিবারদের সংখ্যা বাদই দাও, ওটা পৌরাণিক। এই তো সেদিনের ইতিহাস, মুর্শিদাবাদের নবাব সরফরাজ খাঁর নাকি সতেরোশো বেগম ছিল। তবু সরফরাজ রাবেয়া বেগমকে বেশী ভালবাসতেন। ভালবাসা একটা বিচিত্র মনের অবস্থা ও একবার জন্মালে আর মরে না, অনন্তমূলের মত মানুষের সমস্ত অন্তর জুড়ে মূল বিস্তার করে দেয়। কখনও কখনও অনাবৃষ্টির সময় মনে হয় বুঝি এবার শুকিয়ে গেছে, নিঃশেষ হয়ে গেল। কিন্তু এক পশলা বৃষ্টি পড়লেই সারা অন্তর জুড়ে তার সবুজ অঙ্কুরের ডগা বেরিয়ে আচ্ছন্ন করে দেয়। এই ভায়লা বা ভায়লেট মেয়েটাকে সেই ভালবাসায় ভালবেসেছিলেন দেবেশ্বর রায়। তাই রাঙাপিসী যিনি তাঁর খেলার সঙ্গী ছিলেন, বড় বোনের মত ছিলেন, প্রিয় সখীর মত ছিলেন, তাঁর কাছে লিখেছিলেন—পিসী, তুমি আমাকে হাজার কয়েক টাকা ধার দাও। আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করে রাখছি, টাকা আমি শোধ দেব-দেব-দেব।
তখন ঘটনাটা অনেক দূর এগিয়েছে সুলতা। এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়া তাঁর হয়ে গেছে। এলিয়ট রোডে একটা বাড়ী খাড়া করেছেন। এই বাড়ীটা গোপালদার সঙ্গে পরামর্শ করে করেছেন। জানবাজার থেকে রিপন স্ট্রীট বেশী দূর নয়, তার ওদিকেই এলিয়ট রোড। ফিরিঙ্গী পাড়া। পাড়াটায় যারা বাস করে, তারা খেটে-খুটে খায়, আবার ইংরেজ যখন কলকাতা পত্তন করেছিল, তখন জাহাজে করে পুরুষদের সঙ্গে অনেক মেয়ে যারা এখানে হোটেল, বারে এবং নানা বৃত্তি করে জীবিকা উপার্জন করত, তাদের অনেকে থাকত, তাছাড়া ক্লাইভের আমল থেকে যেসব নবাব ইংরেজরা হারেম রাখত, তাদের বংশের ছেলেমেয়েরাও অনেকে এদিকপানে ছিটকে এসেছিল। লালবাজার, বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট থেকে ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, পার্ক স্ট্রীট, ওয়েলেসলি হয়ে বেনিয়াপোখ়া পর্যন্ত যে সমাজটা, সে সমাজের মধ্যে এক পুণ্যবতী রাণী রাসমণির দৌলত আর সাহসে কিছু এদেশী মানুষ, এদেশী সমাজ কোনমতে টিকে ছিল। আজও আছে। এখন বিক্রম অবশ্য আমাদের বেশী। সেকুলার স্টেটের সুনাম ক্ষুণ্ণ না করেই বেশী হয়ে উঠেছে।
যাক গে।
এই এলিয়ট রোডের বাড়ীখানা ভাড়া নয়, লিজ নিয়ে ভায়লেটকে এনে রেখেছিলেন দেবেশ্বর রায়। এবং পরমানন্দে মধুযামিনী যাপন শুরু করলেন। দিন-রাত্রি, কীর্তিহাট, বাপ-মা, বংশ-পরিচয় সব ভুলে এই ষোল বছরের কন্দর্পটি জীবনে বসন্তোৎসব জুড়ে দিলেন। পরীক্ষা হয়ে গেলেও কীর্তিহাটে ফিরলেন না।
বার বার পত্র লিখলেন রত্নেশ্বর রায়। কিন্তু নানান অজুহাতে তিনি যাওয়া ঠেকিয়ে রাখলেন। রত্নেশ্বর রায় তাঁকে বিশ্বাস করলেন।
তখনকার সমাজ এবং বাঙালীর জীবন মনে করলে এটা খুব অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে না সুলতা।
বাঙলাদেশ তখন জাগছে। সব দিক থেকে, উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম চার দিক থেকে যেন বারোটা সূর্য উঠছে।
শাস্ত্রমতে বলে, সূর্য হচ্ছেন বারোটি। বারোটি সূর্য বাঙলাদেশে তখন চারিদিকে প্রভাতের আলো ফুটিয়ে উঠতে শুরু করেছে। তার শিক্ষা পাল্টেছে, ধর্মের চেহারা পাল্টেছে, নতুন ধর্ম জেগেছে, মুসলমান আমলে হিন্দুধর্মের গোঁড়ামি এবং চারিদিকে তোলা আকাশ-ছোঁয়া পাঁচিল বাঙালীরা নিজেরাই ভেঙে ফেলেছে।
বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী তখন ছাপা হয়ে বের হয়েছে। তাতে নবাবনন্দিনী আয়েষা কুমার জগৎসিংহের প্রেমে পড়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র কুমার জগৎসিংহের জাত বাঁচাতে বিয়েটা দিতে পারেন নি, কিন্তু সত্যি বলতে, তিলোত্তমা থেকে নবাবনন্দিনী আয়েষাকে অনেক মহীয়সী এবং সম্ভবত রূপসী মনোহারিণী করে সৃষ্টি করেছেন।
ক্রীশ্চানধর্মের গতি রোধ হয়ে গেছে; বউবাজারে মা ফিরিঙ্গী কালী পথরোধ করেছেন। এদিকে দক্ষিণেশ্বরে এক প্রায় নিরক্ষর ব্রাহ্মণ এসেছেন, তাঁর আশ্চর্য মহিমা। আশ্চর্য সারল্য। আশ্চর্য প্রেম। অপার ভালবাসা।
ব্রাহ্মধর্মের পর পর থাক হতে হ’তে আদি থেকে নববিধান, এবং নববিধান থেকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে চেহারা নিয়েছে।
মিউটিনির পরই নীল বিদ্রোহ হয়ে গেছে। সে বিদ্রোহে বাঙালী হারে নি, জিতেছে। হরিশ মুখার্জির জেল হয়েছে। ফাদার লঙেরও জেল হয়েছে, যশোরের মাগুরা গাঁয়ের ঘোষেরা মাগুরায় বসে ছোট সাপ্তাহিক বের করেছিল, সে কাগজ নিয়ে তারা বাগবাজারে এসে বসেছে। বাঙলা কাগজকে এক রাত্রে ইংরিজী কাগজে পরিণত করে লাটসাহেবের উদ্যত রোষের সঙ্গে পাঞ্জা লড়েছে। তখন রবীন্দ্রনাথ সতেরো-আঠারো বছরের; দ্বিজু রায়, রামানন্দ চাটুজ্জে, আচার্য প্রফুল্ল রায়, আচার্য জগদীশচন্দ্র তখন বাঙলাদেশে অপরিচয়ের মধ্যে বেড়ে উঠছেন। দক্ষিণেশ্বরের যে ব্রাহ্মণের আশ্চর্য তপস্যাচরিত্র সমগ্র পৃথিবীতে বিস্ময়ের সঞ্চার করেছে, তার মহিমা এবং তপস্যার যিনি ধারক-বাহক—দত্তবাড়ীর নরেন দত্ত, স্বামী বিবেকানন্দ, তিনিও তখন ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। বছর কয়েক পরেই তিনি তাঁর গুরু, যাঁকে তিনি My Master বলেছেন, তাঁর সঙ্গে মিলিত হবেন। এ সময়টা সেই সময়।
বাঙালী সে সময় শুধু ধন-সম্পদ খোঁজে না, বিষয়-বিষয় করে গলি-ঘুঁচিতে ঘোরে-ফেরে না, সে আরও অনেক কিছু খুঁজছে। অনেক প্রশ্নও তার মনে জেগেছে। একদিকে সে ওল্টাচ্ছে এদেশের পুরনো ইতিহাস, শাস্ত্র, পুঁথি, বেদান্ত, উপনিষদ, অন্যদিকে সে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের আস্বাদ নিয়েছে। পাশ্চাত্ত্য উপন্যাস, কবিতা পড়েছে। শুধু রেনল্ডের ‘মিস্ট্রি অব দি কোর্ট অব লন্ডন’ নয়, আরও অনেক পড়েছে, স্কট ডিকেন্স পড়েছে। জীবনে তার নতুন আলোকপাত হয়েছে। দেবেশ্বর রায় বেশ একটু ইংরিজী ঘেঁষা লোক ছিলেন। তিনি এই অর্ধ-শ্বেতাঙ্গিনী ভায়লেটের কিশোর জীবনের ভালবাসায় আকণ্ঠ ডুব দিয়ে তার আস্বাদ গ্রহণ ক’রে ভাবছিলেন, কিছু টাকা মূলধন পেলে তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য ক’রে মাইকেলের মত একজন কেউ হবেন!
সেই সময়টায় তিনি মাইকেলের মত দাড়ি-গোঁফ রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। এবং খাঁটি সাহেবী পোশাক পরে ভায়লেটকে পাশে বসিয়ে ফিটনে চড়ে বেড়াতেও যেতেন।
সুলতা, অন্নপূর্ণা-মা সেই রোগশয্যায় আমাকে ডেকে বললেন—দেখ, দেবু তার মৃত্যুর আগে আমার কাছে এসেছিল। বলেছিল রাঙাপিসী, তুমি আমাকে টাকাটা দাওনি, সে হয়তো আমার ভাল-মন্দ বিচার করতে গেলে ভালই করেছ। কারণ ভায়লেট এমনই অশিক্ষিত ছিল এবং এমনই ওয়াইল্ড ছিল যে, আমি তাকে সহ্য করতে পারতাম না। তাতে এর থেকেও অনেক বেশী যন্ত্রণা আমাকে সইতে হত।
অন্নপূর্ণা-মা বলেছিলেন—তখন দেবু মদ প্রায় সব সময়ই খেত। মনের যাতনায় খেত। তবে হ্যাঁ, বুঝতে কেউ পারত না। দেবুর কথাটা শুনে আমার খুব অনুশোচনা হয়েছিল রে। আমি তাকে বলেছিলাম- দেবু, টাকাটা দিতে আমি পারতাম, কিন্তু তোকে যে চিরকালের জন্যে হারাতাম, দেবু।
দেবেশ্বর বলেছিলেন- না পিসী, তুমি হারাতে না আমাকে। আমি তোমার সেই দেবুই থাকতাম। তবে হ্যাঁ, বাবা-মা’র সঙ্গে ঝগড়া হত। সমাজের সঙ্গে হত। তা হত। কিন্তু তা কি আটকানোই গেল রাঙাপিসী? বল, তুমিই বল! গেল! বাবার সঙ্গে প্রতিপদে ঝগড়া হল। প্রতি পদে। যে মানুষটাকে সারা দেশে বললে, এমন ধার্মিক, সুবিচারক হয় না, তাকে আমি নিষ্ঠুর, অত্যাচারী ছাড়া কিছু দেখলাম না। একটা অত্যন্ত হিংস্র মানুষ। উঃ, রাঙাপিসী বাবার এই মনে চেপে রাখা প্রতিহিংসা, আর সময় এবং সুযোগ বুঝে আইনের পথে শোধ তোলা এ যে কি ভয়ানক তুমি কল্পনা করতে পারবে না। জান রাঙাপিসী, বাবার পছন্দ করা মেয়ে বলে কাশীর বউকে আমি কোনদিন পছন্দ করতে পারলাম না। এমন ধর্মবাইগ্রস্ত, স্বামীতে, দেবতায়, ধর্মে তার অচলা ভক্তি, কোনদিন সে আমার উপর জোর খাটালে না, কোনদিন সে আমার একটা অবিচারের প্রতিবাদ করলে না, না পারলাম তার উপর রাগ করতে, না পারলাম তার উপর ঘেন্না করতে, না পারলাম তাকে ভালবাসতে; পিসী, ভালবাসতে গেলে সে ভালবাসা নিলে না, ফেলেও দিলে না, একটু হেসে পাশে সরিয়ে রেখে দিলে। নেড়েচেড়েও দেখলে না।
জানিস সে কেঁদে ফেলেছিল সেদিন। অন্নপূর্ণা-মা বললেন-আমি সেদিনও তাকে বলতে পারলাম না যে, ওরে দেবু, ও কনে দাদা পছন্দ করে নি রে, পছন্দ করেছিলাম আমি। আমার বড় ভাল লেগেছিল মেয়েটিকে; তোর চিঠি পেয়ে আমি তোকে উত্তর দিলাম না, দাদাকেও বিশেষ কিছু জানালাম না, লিখলাম-আমার সঙ্গে মিটমাটের কথা যা চাহিতেছ, তাহার জন্য কলিকাতা যাইতে লিখিয়াছ; কিন্তু তুমি কাশী এস না কেন? তুমি জমিদার, স্বাধীন মানুষ; আমি মেয়েছেলে, পিসেমশায় ছুটি না পাইলে যাইব কেমন করিয়া এবং মিটমাট দুই পক্ষের মধ্যে বসিয়া করিয়াই বা দিবেন কে!
এরই মধ্যে দেখলাম এই মেয়েকে। দশাশ্বমেধ ঘাটে তার দিদিমার সঙ্গে স্নান করতে এসেছে। ফুটফুটে মেয়েটি। কিন্তু সেই বয়সে কি ধর্মনিষ্ঠা আর কি ভক্তি! পরিচয় নিয়ে জানলুম, দিদিমা নদে জেলার জমিদারবাড়ীর গিন্নী, জমিদার থেকেও ব্যবসায়ে ওদের নামডাক খুব বেশী, অবিশ্যি দেশী ব্যবসায়ীদের মধ্যে। মেয়েটি গিন্নীর মেয়ের মেয়ে, মা মারা যাওয়ার পর থেকে দিদিমার কাছে মানুষ হচ্ছে। আমি পরিচয় দিয়ে পিসেমশাইকে নিয়ে কথাবার্তাটা খানিকটা পেড়ে রাখলাম। দাদাকে লিখলাম, “তুমি শিগগির আসিবে। তুমি এলে মিটমাটের কথা সব হইবে।”
দাদা আসতে পারলে না। কমিশনার লাট অনেক কথা লিখলে। রায়বাহাদুর খেতাব দেবেন সরকার, তার তদ্বিরের জন্য এখন দেশ ছেড়ে আসা অসম্ভব। অগত্যা আমি কলকাতা গেলাম। দেখলাম স্টেশনে জানবাজারের গাড়ী এসেছে। কিন্তু একজন গোমস্তা ছাড়া কেউ আসে নি। আমার রাগ হল। আমি জানবাজার গেলাম না, গিয়ে উঠলাম জোড়াসাঁকোয় জ্যেঠামশাইয়ের বাড়ী।
সেখানে গিয়ে খবর শুনলাম, দেবেশ্বর বন্দুকের গুলীতে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে।
অবাক হয়ে গেলাম। দেবু আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে বন্দুকের গুলীতে?
উত্তর শুনলাম—হ্যাঁ।
পিসেমশাই বললেন—তাহলে এখানে নয়। ফিরে গিয়ে গাড়ীতে ওঠ মা। চল্ ওখানে চল্। এই জন্যে কেউ স্টেশনে আসেনি।
জানবাজারের বাড়ীতে গিয়ে অন্নপূর্ণা দেবী এবং বিমলাকান্ত পৌঁছে দেখেছিলেন রত্নেশ্বর রায় বড় সাহেবডাক্তারকে বিদায় করছেন। সাহেব তাঁর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে তাঁর ব্রুহাম গাড়ীতে চড়ছেন। বলছেন—রয়বাবু, It is only luck—only luck—that has saved your boy. Offer your thanks and gratitude to God and God alone. I have not done anything.
অন্নপূর্ণা-মা বলেছিলেন আমাকে, আমি কাশীতে পিসেমশায়ের কাছে ইংরিজী শিখেছিলাম, কিন্তু সাহেবের কথা একবিন্দু বুঝি নি। পা আমার সিঁড়িতে আটকে গেল, আমি উপরে যেতে পারলাম না।
সাহেবকে বিদায় করে দাদা ফিরে এল ঘরের মধ্যে, পিসেমশায় দাঁড়িয়ে ছিলেন ঘরের মধ্যে, তিনি বললেন-তাহ’লে ভয়ের কিছু নেই!
গম্ভীরভাবে কীর্তিহাটের রায়রাজা আমার দাদা বললে-না। তবে যা হবার হয়ে গেলেই তো ভাল হত। ভগবান আমাকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচাতেন, রায়বংশকে পাপের হাত থেকে রক্ষা করতেন। গুলীটা চালাতে চেয়েছিল বুকে। বন্দুকটার বাঁট মেঝেতে রেখে নলটা বুকে লাগিয়ে পা দিয়ে ট্রিগার টিপেছে, এখন বন্দুক তো ফায়ারিংয়ের সময় খানিকটা ঝাঁকি দেয়, back push করে, তাইতেই পিছলে গিয়ে গুলীটা বগলের ভিতরে মাংস কেটে বেরিয়ে গেছে। ছররা হলেও ক্ষতি হ’ত, দু-চারটে এদিক-ওদিক ঢুকতে পারত। এ একেবারে বুলেট। সুতরাং জীবনহানি হয় নি, কেলেঙ্কারিই সার হয়েছে।
আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিলাম। নড়বার শক্তি তখনও আমার হয়নি। পিসেমশাই বললেন—কি বলছ তুমি রত্নেশ্বর?
—ঠিক বলছি। আমি বাল্যকাল থেকে আঠারো বছর পর্যন্ত আপনার কাছে মানুষ হয়েছি। আপনি কি আমাকে এমনিই মমতাহীন পাষণ্ড করে গড়ে তুলেছিলেন যে, নিজের জ্যেষ্ঠ সন্তান, প্রথম সন্তান সম্পর্কে এমনি কথা বলব? মরাই ওর উচিত ছিল, চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু ওর দুর্ভাগ্য, রায়বংশের দুর্ভাগ্য, সব থেকে বেশী দুর্ভাগ্য আমার যে,
হঠাৎ চুপ করে গিয়েছিল দাদা। বলেছিল-চলুন ওপরে চলুন। এখানে লোকজনে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। বাড়ীর গোপন কথা, কি কেলেঙ্কারির কথা সে এক রকম ওরা জেনেছে, তার প্রতিবিধান তো করতে হবে। কিন্তু আমাদের কথাগুলো ওদের শুনতে দিয়ে লাভ কি?
***
অন্নপূর্ণা-মা থাক-থাক করে চিঠিগুলো সাজিয়ে হাতে ধরে বসে কথাগুলি বলছিলেন আমাকে। ঘরের মধ্যে ছিল শুধু অর্চনা, আর কেউ ছিল না। আমি অনেকটাই জানতাম, কিন্তু এমন বিশদভাবে জানতাম না। বাইরেটা দেখে যতটা জানা যায় ততটাই। মর্মকথা নয়।
দাদা জানবাজারের বাড়ীতে সেবার এসে উঠেছিল খবর-টবর না দিয়ে। খবর যা ছিল, তাতে দাদার আসবার কথা একদিন পরে, কিন্তু মেদিনীপুর থেকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট চিঠি দিয়ে একদিন আগে আসতে বলেছিলেন। বলেছিলেন, চুঁচড়োতে কমিশনার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতেই হবে। সাহেবের কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট যাবে, সেটা দেখাবেন। কমিশনার নিজেই ডেকেছেন।
রত্নেশ্বর রায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গেই সকালে রওনা হয়ে হাওড়া পৌঁছে ওখান থেকেই গিয়েছিলেন চুঁচড়ো। বর্ধমান ডিভিশনের কমিশনারের আসন চুঁচড়োতে। সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করে খুশী মনেই ফিরছিলেন। মনের মধ্যে ক্রোধের আগুন একটা জ্বলছিল। কিন্তু সেটাকেও তিনি লণ্ঠনের ফানুস পরিয়ে আগুন থেকে সুন্দর একটি লণ্ঠন করে তোলা যায় কিনা ভাবছিলেন। সেটা ভায়লেট এবং গোপালকে নিয়ে। ভায়লেট একদা অদৃশ্য হয়েছে কীর্তিহাট থেকে। গোপালই এনেছিল কীর্তিহাট থেকে। এবং দিনকয়েক থেকে একদিন ওই গোয়ানপাড়ারই এক আধবুড়ী গোয়ানবুড়ীকে সঙ্গে নিয়ে ভায়লেটকে এনে তুলেছে এই এলিয়ট রোডের বাড়ীতে। বাড়ীখানা তখন সদ্য নতুন তৈরী হয়েছে। ঝকঝকে বাড়ী। বাড়ীটা করেছিল একজন খাঁটি সায়েব, যার মতলব ছিল-আর হোমে সে ফিরবে না। সেও এক প্রেমের ব্যাপার। এখানে প্রেমে পড়েছিল, তাই ফিরে যাবে না মতলব করেছিল। সেখানে পুরনো বিয়ে করা বউ ছেলেমেয়ে ছিল, একে নিয়ে হোমে গেলে জেল খাটতে হবে। কিন্তু তার ভাগ্য, বাড়ী-টাড়ী হল কিন্তু যে মেয়েটার প্রেমে পড়েছিল, সে মরে গেল হঠাৎ। সায়েব বাড়ীটা বিক্রী করে দিয়ে বিলেত চলে গেল। বাড়ীটা কিনেছিল কলকাতার বাড়ীভাড়া ব্যবসায়ী যারা তাদের একজন। কিন্তু ভাড়া সহজে হচ্ছিল না। বাড়ীটার নাম রটে গিয়েছিল অপয়া-আনলাকী। গোপাল ঘোষ খবর পেয়ে দেবেশ্বর রায়কে খবরটা দিয়েছিল; তরুণ দেবেশ্বর বলেছিলেন-রাবিশ! অপয়া! আনলাকী! ওসব আমি মানি নে গোপালদা। চল, বাড়ীখানা দেখে আসি। পছন্দ হলে ওই বাড়ীই নেব। নতুন বাড়ী, সায়েবী-রুচিতে করা বাড়ী।
তরুণ দেবেশ্বরের দেখবামাত্র ভাল লেগেছিল এবং সেই পথেই বাড়ীওয়ালার সঙ্গে কথা বলে পাকা করে, ওখান থেকেই গিয়েছিলেন, হ্যামিল্টনের বাড়ী। হাতে আংটি ছিল। একটা খুব দামী হীরের আংটি, সেটা পৈতের সময় পেয়েছিলেন; আর একটা আংটি—সেটা বীরেশ্বর রায়ের একটা দামী দুর্লভ নীলার আংটি। সেটা তাঁর আঙুলে শেষদিন পর্যন্ত ছিল। লোকে বারণ করত, এটা পরবেন না। কিন্তু তিনি তা ছাড়েন নি। আংটিটার গল্প ছেলে বয়স থেকে শুনেছিলেন দেবেশ্বর রায়। এ নীলা সহ্য হলে রাজা হয় মানুষ। এই আংটিটা একদিন বাপের সম্মুখেই খোলা জহরতের বাক্স থেকে হাত-সাফাই করে তুলে নিয়েছিলেন। সেটা পরতেন তিনি। এবং ভায়লেটকে পেয়ে তাঁর ধারণা হয়েছিল আংটিটা তাঁর সহ্য হয়েছে। হ্যামিলটনের বাড়ীতে গিয়ে বড় হীরের আংটিটা এবং হীরের বোতাম বিক্রী করেছিলেন, আর এই নীলাটা বন্ধক রেখে টাকা কম পাননি—পেয়েছিলেন দশ হাজারের বেশী।
সেই টাকায় বাড়ী লিজ নিয়ে ফার্নিচার কিনে সাজিয়ে-গুছিয়ে ভায়লেটকে কীর্তিহাট থেকে এনে মধুচন্দ্রিমা যাপন করছেন।
দেবেশ্বর রায় বাপ রত্নেশ্বর রায়কে ভয় করেন। কিন্তু অন্তরে অন্তরে বাপের কঠোর সমালোচক। বাপের কাঠিন্য এবং কঠোরতা তাকে তাঁর অজ্ঞাতসারে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। তাছাড়া তিনি বেপরোয়া। তিনি গ্রাহ্য কাউকে করেন না। বাপকে পত্রে লেখেন—তখনকার দিনের এ-মিটিং ও-মিটিংয়ের কথা। এবং তার সঙ্গে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজের মতের কথাও জানাতেন। যা পড়ে রত্নেশ্বর মৃদু হাসতেন। তাঁর মনে পড়ত তাঁর বাল্যকালের কথা। তিনি যখন নিজেকে কীর্তিহাটের রায়বাড়ীর দৌহিত্র বলে জানতেন, তখন তিনি নিত্য অভিসম্পাত দিতেন এই বংশটিকে। সোচ্চারে দিতে পারতেন না ভবানী দেবীর জন্য। ভবানী দেবীকেও তিনি তখন নিজের গর্ভধারিণী বলে জানতেন না।
তারপর?
তারপর বিচিত্র ঘটনাচক্রে সব উল্টে-পাল্টে গেল। বীরেশ্বরের পুত্র হিসাবে তিনি আজ কীর্তিহাটের ষোল আনা সম্পত্তির একচ্ছত্র মালিক। তিনি নিজের মত অনুযায়ী বীরেশ্বর রায়ের আমলের ধারাপদ্ধতি সবই পাল্টেছেন। জোরজুলুম, জবরদস্তি, দৈহিক নির্যাতন করে, গ্রাম জ্বালিয়ে, লাঠিবাজী ক’রে প্রজাশাসন তিনি তুলে দিয়েছেন। আজ সবই চলে দেশের প্রচলিত আইনের কাঁটায়-কাঁটায়। কারুর সাধ্য নেই যে তাঁকে প্রজাপীড়ক বলে, তবু তিনি নিজে জানেন, অনুভব করেন আজ কীর্তিহাটের কাছারীকে কীর্তিহাট এস্টেটের প্রজারা কত বেশী ভয় করে। এ তো সেই তিনিই করেছেন। এবং তার সঙ্গে দেশের আমল-হাল-চাল আইন সাহায্য করেছে।
১৮৫৭ সাল থেকে ভাইকাউন্ট আর্ল ক্যানিং, লর্ড এলগিন, লর্ড লরেন্স, লর্ড মেয়ো, লর্ড নর্থব্রুক, লর্ড লিটন একের পর এক লাট হয়ে এসে গোটা দেশে কেমন করে রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করলে তা দেখেছেন তিনি। শিখেছেন অনেক কিছু। লর্ড লিটন চলে যাবেন, আসবেন লর্ড রিপন। লর্ড লিটনই তাঁকে রায়বাহাদুর খেতাব মঞ্জুর করেছেন।
ছোট লাটবাহাদুর নিজে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি লিখেছেন—“তুমি যে তোমার জমিদারীর মধ্যে নেটিভ ক্রীশ্চানদের জন্য চার্চ করেছ এবং সেখানে স্কুল ক’রে দিয়েছ তাদের জন্য, এর জন্য তোমাকে আমার ব্যক্তিগত ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ-ধরনের উদারতা সত্যই প্ৰশংসনীয়।”
দেবেশ্বর আজ চিঠিপত্রে যাই লিখুক কলকাতার মিটিং এবং হুজুগ আর ফ্যাশনের নেশায় তার বিন্দুমাত্র লেশ থাকবে না, যখন সে রায়বাড়ীর জমিদারীর আসনের স্বাদ পাবে। তার আয়ের স্বাদ, সম্মানের—তার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মূলের সন্ধান পাবে। হ্যাঁ, তবে নতুন জীবনে এগুলো ভাল। অন্তত সমাজে, বাইরে পাঁচজনের সামনে ভাল লাগে।
তিনি জানতেন না, দেবেশ্বর নিজের জীবনে কতখানি শিকড় চালিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে দুনিয়ার মাটির উপন। বুঝতেন না তার মতামতের মূল্য কতখানি! এবং মনে তিনি ভাবতেও পারেন নি যে, দেবেশ্বর বোল বছর বয়সে চৌদ্দ বছরের ভায়লেটের প্রেমে পড়েছে এবং গোপালদার সাহায্যে তাকে কলকাতায় নিয়ে এসে বাড়ী ভাড়া করে রেখেছে।
রত্নেশ্বর রায়ের অনুমান ছিল এবং কীর্তিহাট অঞ্চলে প্রবল গুজব ছিল যে, গোপালই ভায়লেটকে নিয়ে পালিয়েছে কলকাতায়। রত্নেশ্বর চিঠি লিখেছিলেন কলকাতায়, নায়েবকে—“গোপাল সম্পর্কে এখানে অনেক গুজব রটিয়াছে। সে কলিকাতায় কি করিতেছে বা তাহার সমুদয় বিবরণ আমাকে পত্রপাঠ জানাইবা।” দেবেশ্বরকে লিখেছিলেন—
He is a scoundrel—The Goans of our Goanpara say that Gopal has eloped with Violet Pedros the girl-who you may remember-garlanded us in the meeting and who happens to be the daughter of one of our women employees in the house-Anjana. You were a mere boy at that time, she was your nurse-very favourite of yours-you may remember her. She embraced christianity and married a Goanese Christian. Violet is her daughter. You just warn him-and tell him-that he shall have to be a Christian and marry this girl.
***