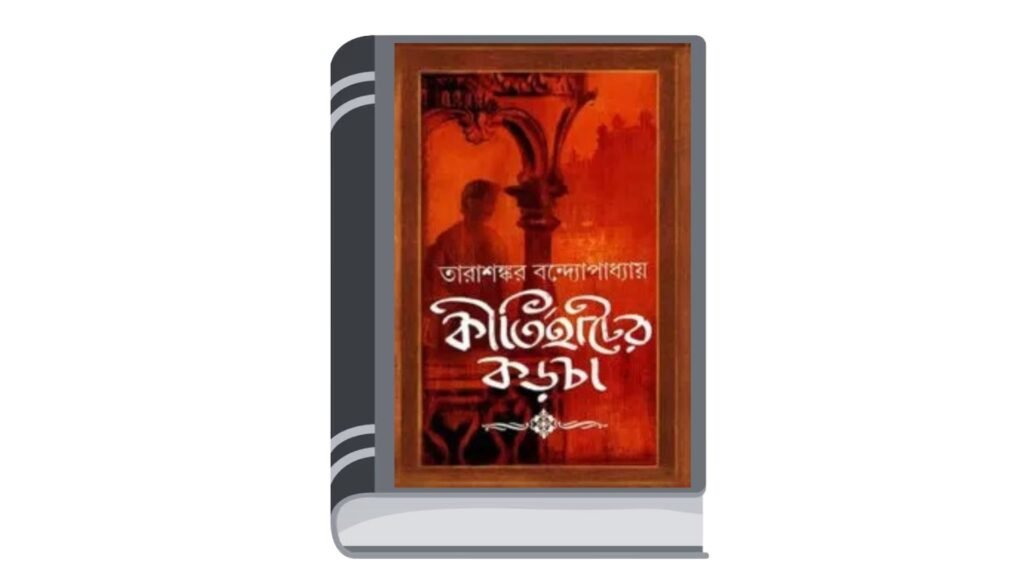কীর্তিহাটের কড়চা – ৪র্থ খণ্ড – ১৮
১৮
শুধু ঘুম নয়, আনন্দ-উল্লাস এ সমস্তই যেন ওই হারা রে আমার অপহরণ করে নিয়েছিলেন। আমার পিছনে তিনি যেন অশুভ শনিগ্রহের মত অথবা কলির মত ফিরতে শুরু করেছিলেন। অথবা রায়বংশের প্রেতাত্মার মত ফিরতে শুরু করেছিলেন।
ওই ঘটনার ঠিক একদিন পর তিনি আবার এসেছিলেন হোটেলে। এবার একা নয়—সঙ্গে একটি সুন্দরী তরুণী।
আশ্চর্য সুলতা, আমি কার্ড পেয়ে তাঁকে ফিরিয়ে দিতে পারি নি। ঘরে এলেন সে মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে। আমি তার মুখের দিকে তাকালাম। আমার দেহের রক্ত চঞ্চল যেমন হয়ে উঠল, তেমনি একটা নিদারুণ আতঙ্ক আমার বুকের মধ্যে একটা অসহনীয় উদ্বেগের সৃষ্টি করলে।
উইন্ড হলে হার্টের উপর প্রেসার পড়লে যেমন হয়, ঠিক তেমনি। তারিখটা স্মরণীয় তারিখ, থার্ড সেপ্টেম্বর নাইনটিন থার্টি-নাইন। জার্মানীর বিরুদ্ধে ইংরেজ ওয়ার ডিক্লেয়ার করবে, তার আগে, এগারটা পনের মিনিটে প্রাইম-মিনিস্টার মিস্টার চেম্বারলেন রেডিয়োতে বক্তৃতা দিচ্ছেন। ১লা সেপ্টেম্বর জার্মানী পোলান্ড আক্রমণ করেছে ভোরবেলা। নেভিল চেম্বারলেনের বক্তৃতা শুনছিলাম আমি। হারা রে ঘরে ঢুকলেন, সঙ্গে মেয়েটি।
বললেন—I have come Mr. Roy. Let me introduce Miss Laura Knight to you-She is more than my own daughter-my disciple, a fan of mine. And Laura-this is Mr. Ray-S. Ray-an artist, a famous artist-and a very learned man-also a very rich man. You see those two pictures on the wall-one a mother and another a darling. But the girl is the same, you see-this is tantra of India. The Eternal Mother and the Eternal She, they are one and the same.
আমি আর সহ্য করতে পারি নি। আমি বলেছিলাম—Will you please stop Mr. Ray! মিস্টার হারা রে বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন—You don’t like Miss Knight? She is very intelligent with a very soft and sweet mind-she wanted to work as your secretary.—
আমি বলেছিলাম-বাংলায় বলেছিলাম, দয়া করে আপনি চলে যান—আমি জোড়হাত করছি মিস্টার রে—
সুলতা, মেয়েটির মুখে যেন রায়বংশের আদল দেখতে পাচ্ছিলাম। থরথর করে কাঁপছিলাম আমি।
—কি হল মিস্টার রায়? আপনি অসুস্থ?
আমি এবার চীৎকার করে বলেছিলাম—Get out I say get out–
রেডিয়োতে তখনও প্রাইম মিনিস্টার মিস্টার চেম্বারলেনের বক্তৃতা চলছে। সারা ইংল্যান্ডের লোক বোধহয় তখন কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত নির্বাক হয়ে গেছে। যুদ্ধ! আবার সর্বনাশা যুদ্ধ বাধল!
হারা রে বললেন—কিছু টাকা ওকে দাও রায়, ওকে আমি নিয়ে এসেছি তোমার নাম করে। অনেক প্রত্যাশা করে এসেছে—She must get something. Mr. Ray—please!
আমি বললাম- She is your daughter!
চমকে উঠলেন হারা রে, বললেন–কে বললে?
—ওর মুখ বলছে।
—তোমার দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ রয়, কিন্তু She is a good girl and beautiful also—is she not?
এতক্ষণে মেয়েটি কথা বললে—Give me my dues. বলে সে আমার সিগারেটের টিন থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লে।
আমি ওদের বিদায় করলাম। মূল্য ভালই দিতে হল। কিন্তু তাতে আমার দুঃখ ছিল না। বরং আসবার সময় ওদের আরও কিছু পাঠিয়ে দিয়ে এসেছিলাম। হারা রে মিথ্যা কথা বলেন নি; ঋণ তাঁর অনেক, আকণ্ঠ ডুবে আছেন বললে মিথ্যা বলা হয় না।
দেশে ফিরবার টিকিটের দাম আর পথ-খরচ রেখে বাকিটা হারা রে-কে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।
দেশে ফিরেছিলাম মাসখানেকের মধ্যেই। ও-দেশে থাকতে আর সাহস হয় নি। লোকে বলেছিল—যুদ্ধের ভয়ে পালাচ্ছি কিন্তু তা নয়, আমি পালিয়েছিলাম হারা রে-র ভয়ে এবং তাঁর মেয়ে শম্পা রে-র ভয়ে।
মেয়েটার নাম লরা নাইট নয়। ওর নাম শম্পা রে। ওদের ভয়ে আমি পালিয়ে এলাম।
কথা বলতে বলতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে খানিকটা পায়চারি করে সুরেশ্বর যেন দম নিয়ে বললে—সাত পুরুষ ধরে কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্য থেকে সুরেশ্বর রায় পর্যন্ত যত কলঙ্ক রায়বংশ অর্জন করেছে, সুলতা, তার মধ্যে এই হারা রায়ের কলঙ্কের চেয়ে কালো এবং নীরেট অর্থাৎ ওজনে গুরুভার কলঙ্ক আর কেউ অর্জন করে নি।
বলতে বলতে, বলতে পারি নি; দিনের আলো ফুটছে, লজ্জাবোধ করছিলাম; কিন্তু না, বলব, না বললে রায়বংশের মুক্তি নেই। খবরটা জেনেছিলাম জাহাজে উঠে। জাহাজে উঠে হঠাৎ দেখা হল একটি মহিলার সঙ্গে। আমি জাহাজে যখন উঠলাম তখন মহিলাটি ডেকের উপর দাঁড়িয়েছিলেন অন্যমনস্ক ভাবে। উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। পোশাক দিয়ে বোঝা গেল ভারতবর্ষের মেয়ে; তার কিছুটা পরিচয় চুলে এবং চোখে আছে; নইলে রঙ দেখে ধরা যায় না। সাদা পাড়হীন শাড়ী এবং ব্লাউজ দেখা যাচ্ছিল বোতাম খোলা ওভারকোটের ফাঁক দিয়ে। বয়স হয়েছে, বয়স চেহারাকে খানিকটা ভারী করে। আমার মনে হল যেন চেনা মুখ। একদিন পর তিনি নিজেই এসে আমার সঙ্গে দেখা করে চেনা দিলেন—পরিচয় ঝালিয়ে নিলেন। এবং হারা রে’র কথা তিনিই বললেন।
ইনি অন্য কেউ নয় সুলতা, ইনি সেই ‘চন্দ্রিকা’। যাই তিনি করে থাকুন, পরিচয় তাঁর যাই হোক, তিনি আমার মাতৃতুল্যা। প্রথমটা জাহাজে তাঁকে দেখে আমি খুশি হই নি, সন্তুষ্ট হই নি। শুধু ভেবেছিলাম আমার ভাগ্যের কথা। আমি তাঁকে চিনতেও চাই নি কিন্তু তিনি আমাকে চিনলেন। আমি চিনি না বলতে পারলাম না। দেখলাম যেন তিনি অনেকটা পাল্টে গেছেন। তিনি এখন সম্পূর্ণরূপে জীবনে নিস্পৃহ এবং উদাসীনা হয়ে উঠেছেন। বাবার মৃত্যুর পর একবার মাত্র দেশে গিয়ে আমার মায়ের সঙ্গে দেখা করে বাবার কিছু কাগজপত্র মাকে দিয়ে এসেছিলেন। মা আমার সে ধাক্কা সহ্য করতে পারেন নি। তাতেই তিনি মারা গিছলেন। মা’র মৃত্যুখবর কলকাতাতেই পেয়েছিলেন তিনি কিন্তু এরপর আর তিনি ফিরে এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারেন নি। এবং ভারতবর্ষ থেকে পালিয়ে এসেছিলেন এ দেশে। আবার এতকাল এ দেশে কাটিয়ে এবার ইন্ডিয়ায় ফিরছেন। বহুদিন থেকেই ফিরবেন ইচ্ছা ছিল, এবার এই যুদ্ধ লেগেছে বলে ফিরবার একটা তাগিদ পেয়ে গেছেন।
***
তিনি হারা রায়কে চিনতেন। জাহাজে তখন সর্বদাই সবার মনে একটা আতঙ্ক ছাইচাপা আগুনের মধ্যে চাপা রয়েছে। একটা উত্তাপ অহরহ অনুভব করে। তাই প্রতিটি যাত্রীই সঙ্গী বন্ধু খুঁজে ফেরে, সামান্য অন্তরঙ্গতায় মানুষকে আপনজন ভাবতে চায়। জার্মান ইউ বোট তখন বাহির দরিয়ায় বেরিয়ে পড়েছে হাঙ্গরের মত, তবে তার গতিবিধি তখনও উত্তর মাথায় নরওয়ে সুইডেনের উপকূল এবং উত্তর সমুদ্র হয়ে আটলান্টিকের দিকে। একদিকে ফ্রান্স, অন্যদিকে ইংল্যান্ডকে রেখে নিচের দিকে তখনও নামে নি। এই অবস্থায় চন্দ্রিকা মালহোত্রা আমার কাছে আসতেন, আমাকে মাই সন বলে ডাকতেন—আমি তাঁকে ফিরিয়ে দিতে পারি নি।
শুধুই বসে পৃথিবীর অবস্থা নিয়ে কথা হত প্রথম প্রথম। এরই ফাঁকে ফাঁকে দু’-চারটে আমার বাড়ীর কথা আমার ব্যক্তিগত কথা জিজ্ঞাসা করতেন।
একদিন প্রশ্ন করলেন—ইউ হ্যাভ নট ম্যারেড?
বললাম–না।
কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—এইবার বিয়ে কর! বললাম না।
বললেন—কেন?
উত্তর দিতে গিয়েও দিলাম না, দিতে পারলাম না যে বাবা তাঁর শেষ চিঠিতে বলে গেছেন—যেন আমি বিয়ে না করি।
একদিন বললেন—তুমি এতে ভেসে যাবে না?
বললাম—না। তা মনে করি না। এখনও অন্তত যাই নি।
—মনে কর না? খুব ভাল। এই জোর যেন শেষ পর্যন্ত রেখো। একটু চুপ করে থেকে বললেন-দেখ, তোমার বাবাকে আমি ইচ্ছে করেই টেনেছিলাম—আমিই অপরাধিনী। তিনি ঠিক ছিলেন না। আই ওয়াজ দি ম্যাগনেট। প্রথমটা কষ্ট পেয়েছিলাম আকর্ষণ করতে। কিন্তু একবার যখন তিনি আমার আকর্ষণে সংসার থেকে ছিঁড়ে বের হলেন তখন তিনি যেন শুটিং স্টার। তাঁকে ধরে রাখা যায় না—গেল না!
চুপ করে রইলাম।
তিনি এইবার বললেন-তোমার বাবার কাছে তোমাদের বংশের গল্প শুনেছি কিছু কিছু। বলতেন—একটা কি অভিশাপ আছে তোমাদের বংশে। আমি বিশ্বাস করি নি-হেসেছি। পৃথিবীতে ম্যান এ্যান্ড উয়োম্যান এদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ নেচার’স ল। একটি পুরুষ একটি নারীকে দেখলেই হি উইল শো হিমসেলফ্ অ্যান্ড শী উইল ট্রাই নট টু লুক অ্যাট হিম, বাট শী উইল লুক অ্যাট হিম। তার উপর যেখানে পুরুষের হাতে সম্পদ জমা হয়েছে সেখানে সে জিততে না পারলে কিনবে। কিন্তু তার থেকেও তোমাদের মধ্যে কিছু বেশী আছে। তোমাদের আর একজনকে দেখেছি আমি ইংল্যান্ডে। তাকে দেখলে আমার ভয় হয়। একজন বড় পণ্ডিত এবং আশ্চর্য হিপনটিক পাওয়ারের অধিকারী। সম্ভবত সম্পর্কে তোমার খুড়ো—
—আর ইউ স্পীকিং অব হারা রে?
সবিস্ময়ে চন্দ্রিকা বললেন—তুমি জান তাকে? দেখেছ?
বললাম- দেখেছি।
—কতটুকু দেখেছ কতটুকু জেনেছ? গ্লাস-কেসের মধ্যে কিং কোব্রা দেখা এক কথা সুরেশ্বর, আর বনের মধ্যে তাকে খোলা অবস্থায় দেখা আর এক কথা। তুমি তাকে গ্লাস-কেসের মধ্যে দেখেছ। হয়তো বা তোমার সত্য পরিচয় না জেনে তোমার কাছে তার সেই বহুবার পুনরাবৃত্তি করা মিথ্যা পরিচয় দিয়ে ভিক্ষে চাইতে এসেছিল। বলেছিল- হাজার বছর আগে তার পূর্বপুরুষেরা রাজা লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী ছিলেন।
বিষণ্ণ হেসে বললাম—হ্যাঁ। বলতে এতটুকু বাধল না।
—বাধে না। ওই পরিচয়টাকে সত্য করে তুলেছে হারা রে। লোকে মিথ্যে জেনেও আবার ওটাকে সত্য বলে মানতে চেষ্টা করেছে। তারপর হয়তো উপনিষদের শ্লোক শুনিয়েছে, গীতা শুনিয়েছে—ইয়োরোপীয়ান ফিলজফিতেও পণ্ডিত হারা রে। কিন্তু সে তার পরিচয়ের কতটুকু? বারতিনেক সে জেল খেটেছে—
এবার আমি বললাম—আন্ট চন্দ্রিকা, মিস মালহোত্রাকে এই নতুন করে পরিচয় হয়ে আস্ট বলতাম, মিস্ মালহোত্রা বলতে কেমন লাগত; বললাম—আন্ট চন্দ্রিকা, তিনি তাঁর মেয়েকে নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন, যার নাম বলেন লরা নাইট; কিন্তু যার আসল নাম শম্পা রায়।
চমকে উঠলেন আন্ট চন্দ্রিকা। বললেন—দেখেছ তুমি তাকে?
—দেখেছি। তার মুখের মধ্যে রায়বংশের মুখের আদল দেখেছি।
একটু চুপ ক’রে থেকে চন্দ্রিকা দেবী আবার বললেন—ওটা তুমি ভুল দেখেছ। অথচ আদল যদি সত্য হয় তবে সেটা অ্যাকসিডেন্টাল। কিন্তু ট্রুথটা আরও ভয়ঙ্কর।
স্থিরদৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম উত্তরের অপেক্ষায়। চন্দ্রিকা দেবী বললেন—তুমি জান কিনা জানি না-এক সময় এক অ্যাকট্রেসের সঙ্গে অবৈধ প্রেম করেছিল হারা রে এবং তার জন্য জেলে গিয়েছিল।
বললাম—জানি।
চন্দ্রিকা বললেন—লরা নাইটই মেয়েটার আসল নাম। ওকে কোলে নিয়েই ওর মা সদ্যবিধবা অবস্থায় হারা রে-র দৃষ্টিতে পড়েছিল এবং প্রেমে পড়েছিল। কিন্তু
—কি কিন্তু–?
—মেয়েটার নাম ছেলেবেলায় হারা রে-ই পাল্টে দিয়েছিল। বলত-শম্পা। তারপর এখন লোকে বলে—সে তার মিসট্রেস!
চমকে উঠেছিলাম শুনে। বলছ কি তুমি?
—সত্য বলছি। ওকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ও তোমার কে? কি নাম ওর? লরা নাইট না শম্পা রায়? শয়তানের হাসি হেসে হারা রে বলেছিল—“যা তোমার মনে হবে তাই। তাই মনে করতে পার। অথবা বলতে পার both —আমার ঔরসে ওর জন্ম নয়, কিন্তু তার থেকে বেশী ওকে মেয়ের মতই মানুষ করেছি এক সময়। কিন্তু তাতে কি? পৃথিবীতে প্রকৃতি আর পুরুষ ছাড়া কিছু নেই। ম্যান অ্যান্ড উয়োম্যান—ইটারনাল হি অ্যান্ড শী; সুরেশ্বর আমি উয়োম্যান—ইটারনাল ওকে কটু কথা বলে ধমকাতে চেষ্টা করেছিলাম, হারা রে শয়তানের মতো হা-হা করে হেসে বলেছিল—তুমি-তুমি বুঝতে পারবে না। বুঝবে না তুমি! রাজাদের ইতিহাসে এ তুমি পাবে, তান্ত্রিকদের তন্ত্রে এর বিধান আছে। আর যদি তুমি মিথ্যে সমাজ-শাস্ত্রের গণ্ডী পার হতে পার তবে বুঝতে পারবে, এসব মিথ্যে সব মিথ্যে। আমি তান্ত্রিকের বংশ, আমি ভূমির অধিকারীর ছেলে—আই ক্যারি রয়াল এ্যান্ড তান্ত্রিক সাধকস ব্লাড ইন মাই ভেনস।”
মিস মালহোত্রা বলে যাচ্ছিলেন—আমি শুনতে শুনতে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম।
মানুষের ইতিহাস একদিকে যত আলোকোজ্জ্বল অন্যদিকে তত অন্ধকার; গাঢ়তম চরমতম অন্ধকার, এ নিয়ে বিতর্ক নেই। কিন্তু তবু মানুষ ওই আলোকোজ্জ্বল দিকটার দিকে তাকিয়েই বেঁচে আছে, সেইটেকেই সে স্বীকার করে। হারা রায়ের মত অন্ধকারকে।
মনে আছে সুলতা—হারা রায়কে অভিসম্পাত দিতে গিয়ে চমকে উঠেছিলাম; মনে পড়ে গিয়েছিল শ্যামাকান্তকে। ভবানী দেবী রায়বংশে বধূ হয়ে এসেও শ্যামাকান্তের তামস তপস্যার ধারাকে বিশুদ্ধ করতে পারেন নি।
সুলতা, নিজের উপর একটা অবিশ্বাস জন্মে গেল। রাত্রে জাহাজে শুয়ে চোখ বুজলেই ওই অন্ধকার আমাকে চেপে ধরত। আমি ভয় পেতাম।
ডেকে মেয়েদের দেখতাম। জাহাজটায় ভারতীয় যাত্রীর ভিড় বেশী; বেশ কয়েকজন মহিলা যাত্রীও ছিলেন। নির্বিঘ্নে সুয়েজ পার হবার পর থেকেই সকলের উল্লাসই বেড়ে গেল। মেয়েদের বেশী। বিলেত থেকে নতুন জাত নিয়ে ফিরছেন তাঁরা। বিলেতের মুক্ত হাওয়ার দমকায় তাঁদের মাথার ঘোমটাই শুধু খসে নি, তাঁরা বেশবাসকে বেশ খানিকটা অসম্বৃত করে উতলা সমুদ্রবাতাসে নতুন যুগের ধ্বজার মত উড়িয়ে ফিরছেন।
আমি ভয়ে কারুর সঙ্গে মিশি নি। মিশতে চাই নি। কেবিনের মধ্যে রঙ তুলি নিয়ে বসে থাকতাম। ছবি আঁকার মধ্যে মগ্ন হতে চাইতাম। কিন্তু ছবি আঁকতে গেলেই মেয়ের মুখ তুলির মুখে ফুটে উঠত।
আমি ভয় পেলাম সুলতা। মনে হল আমার, আর বোধ হয় রায়বংশের বাঁচবার অধিকারই নেই।
দিবালোকের মত স্পষ্ট বুঝতে পারলাম একটা সত্য। শ্যামাকান্ত ধর্মসাধনায় যেখানে পৌঁছুতে চেয়েছিলেন পৌঁছেছিলেন, সোমেশ্বর রায় সম্পদের জোরেও সেখানে পৌঁছেছিলেন, আধুনিক শিক্ষাকে আয়ত্ত করে হারা রেও সেইখানে পৌঁছেছেন। ব্রজদা তোষামুদি শিল্প আয়ত্ত করেও সেখানে পৌঁছুতে চেয়েছিলেন। আমিও ঠিক সেই পথে চলেছি, আমার ছবিতে ফুটে উঠছে নারীর মুখ
বম্বেতে নেমেছিলাম অত্যন্ত ভীত হয়ে। মনে হয়েছিল মানুষের বংশলতার মধ্যে রায়বংশে সেই প্রথম পুরুষ থেকে এ পর্যন্ত যে পথে হেঁটেছে তাতে তার আর বাঁচবার অধিকার নেই। তাতে ছেদ টানতে হবে। অথবা ওই হারা রে-র সত্যকে এবং শ্যামাকান্তের সত্যকে সাহস করে আঁকড়ে ধরে উঁচু গলায় বলতে হবে—“এই সত্যই শ্রেষ্ঠ সত্য বাকি সবই ভ্ৰান্তি। মায়া। মিথ্যা।”
কিন্তু তা পারি নি। আমার কণ্ঠনালীর ভিতর দিয়ে স্বর বের হয় নি, আমার জিভ বাক্যগুলো উচ্চারণ করতে গিয়েও উচ্চারণ করতে পারে নি। আমার মনে পড়ত শ্যামাকান্তের সেই আর্তনাদের কথা। নিজেই নিজের গলা টিপে শ্যামাকান্ত বলতেন, ছেড়ে দে ছেড়ে দে। বলতে দে। বলতে দে।
***
বম্বেতে নেমে মনে হল, কেন এলাম ফিরে?
ইউরোপে যুদ্ধ বেধেছে। হিটলারের বাহিনীর ব্লিৎস ক্রিগের সামনে সমস্ত বাধা ঝড়ের মুখে ধুলোর মত উড়ে যাচ্ছে। ওদিকে পোল্যান্ড থেকে বলকান-এদিকে ফ্রান্স থেকে স্ক্যান্ডেনেভিয়া পর্যন্ত জ্বলছে। ইংল্যান্ডকে মাশুল দিতে হবে। থাকলেই ভাল হত। যেতাম ধুলো হয়ে উড়ে। ইংরেজের পারমানেন্ট সেটেলমেন্টের প্রসাদপুষ্ট বংশের সন্তান, যুদ্ধেও তো লেগে যেতে পারতাম। বিলেতে অনেক ইংরেজীনবিশ বিলিতী সভ্যতামুগ্ধ ভারত-সন্তান যুদ্ধে যোগ দেবার জল্পনা-কল্পনা করছে, তা শুনে এসেছিলাম। আমি তো দুদিক থেকেই যোগ্য। আমি সত্যাগ্রহকে বিদায় জানিয়ে সকল আগ্রহকে হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছি, আমার তো স্থান ছিল ওখানেই
নিজেকে তিরস্কার করেছিলাম সুলতা। এ তুমি ভীরুর মত করলে কি?
বাঁধন-কাটা জীবনের সঙ্গে সুতোকাটা ঘুড়ির কোন তফাত নেই। এখান থেকে একটা বাতাসের তোড়ের মুখে গিয়েছিলাম বিলেতের আকাশে, আবার উল্টো বাতাসে ফিরে এলাম ভারতবর্ষে। এসে একটা হোটেলে বসে ভাবতে লাগলাম বাকী জীবনটা কাটাব কি করে?
কাটা ঘুড়ির সঙ্গে যে সুতোটুকু থাকে তা মধ্যে মধ্যে গাছের ডালে, টেলিগ্রাফের তারে আটকে ঘুড়িটাকে বাতাসের ঝাপটা খেতে দেখেছ? তেমনি মনের অবস্থা।
চন্দ্রিকা মালহোত্রার যাবার কথা দিল্লী। উনি বলেছিলেন কোন একটা চাকরি-বাকরি জুটিয়ে তিনি নেবেন এবং তার উপর নির্ভর করে বাকী জীবন কাটিয়ে দেবেন। সেও যদি ভাল না লাগে তবে ক্রীশ্চান মিশনে মানুষের সেবার কাজ নিয়ে কাটিয়ে দেবেন। বম্বেতে নেমে আমার মনের অবস্থা দেখে উনি আমাকে ফেলে দিল্লী রওনা হতে পারলেন না। যে হোটেলে আমি ছিলাম সেই হোটেলে থেকে গেলেন। আমার মনের অবস্থা উনি অনুমান করেছিলেন, আমার মদ খাওয়া দেখে।
বম্বেতে হোটেলে একটা দিন অত্যন্ত অস্থিরতার মধ্যে সম্ভবতঃ আক্রোশবশেই মদ বেশী পরিমাণে খাচ্ছিলাম। রায়বংশের যে জীবনধারা আমাকে কীর্তিহাট থেকে কলকাতা, কলকাতা থেকে ইংল্যান্ড, আবার ইংল্যান্ড থেকে বম্বেতে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে, যার ভয়ে আমি আতঙ্ক দেখি; মায়ের মরা মুখ ভেসে ওঠে, সেই জীবনধারার জন্যেই যেন আমি পাগল হয়ে উঠছিলাম। আমি জমিদার, রায়বংশের শেষ জমিদার সন্তানের মতই জীবনযাপন করব। কেন করব না? আমার অনেক সম্পদ জমে আছে। আমি প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করে এসেছি বিলেতে। দেশে ব্যাঙ্কে এখনও লক্ষাধিক টাকা আমার মজুত আছে। আমার বিষয় আছে, কলকাতার বাড়ী আছে। যার মূল্য পাঁচ-ছয় লক্ষের উপর।
লক্ষই হোক আর কোটিই হোক, খরচ করে ফেলতে কতক্ষণ? তবে খরচ করতে হলে ওই জমিদার বা রাজার ছেলের মত বাঁচতে হবে। ওই বাঁচার মধ্যেই খরচের পথ আছে। এক কথায় দান করে দেওয়া যায়, সেটা আরও সোজা, কিন্তু হিসেবে সোজা হ’লেও কাজে কঠিন। ঠিক করে ফেললাম ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াব, রায়বংশের ছেলের মতই ঘুরে বেড়াব। ভাঙা প্রাসাদ, পুরোনো কেল্লা, বিরাট মন্দির, মসজিদ, গুহার অভ্যন্তর দেখে বেড়াব আর তার সঙ্গে নারী আর সুরা। তারপর সর্বস্বান্ত হয়ে লিভার পাকিয়ে মরব; কেউ জানবে না পরিচয়; মুদ্দোফরাসে পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে ফেলে দেবে। অথবা দেহটাকে চ্যারিটি করে যাব, লিখে রেখে যাব কোন মেডিকেল কলেজে দিয়ে দিতে। সেইটে হবে আমার লাস্ট উইল। এর থেকে ভাল উইল আর অধিকতর নাটকীয় উইল আর কি হতে পারে একজন রায়বংশের সন্তানের পক্ষে, বল?
সে-কাল হ’লে দেহটা দিয়ে যেতাম বিক্রমাদিত্যের মত কোন রাজাকে। বলে যেতাম—মহারাজ, এই দেহটা তুমি নিয়ো, চিতায় পুড়িয়ো না, জলে ভাসিয়ে দিয়ো না, কবর দিয়ো না, বুকে বসে তান্ত্রিক তপস্যা করো, তোমার সামনে সাক্ষাৎ পরমাপ্রকৃতি আসবেন। তুমি তার কাছে চেয়ে নিয়ো তোমার ইচ্ছামত বর। কোন্ বর? অনন্তকাল পরমায়ু, অমরত্ব? না, তা নিয়ো না।
তবে কি নেবে? কোন্ বর নেবে?
শ্যামাকান্ত শেষ পর্যন্ত মা বলে মুক্তি চেয়েছিলেন। হেরে গিয়েছিলেন। নিজে মুক্তি নিয়ে বংশের মধ্যে নিজের কামনা রেখে গেছেন। সেই কামনা পূর্ণ হবার বর।
সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠতাম। পারতাম না ওই বর চাইবার কথা উচ্চারণ করতে।
***
এতটুকু বাড়িয়ে বলি নি সুলতা।
সমস্ত কথা যথাযথ ভাবে সাজিয়ে পরের পর বলবার মত করে মনে নেই। কারণ সে সময় প্রায় একটা বছর আমি প্রায় দিনরাত্রি মদ খেয়েছি। ইচ্ছে করেই মদ খেয়েছি তাদের
মত করে যারা মদ খেয়ে মরবে বলে সঙ্কল্প ক’রে মদ খায়।
বিষ খেয়ে মরার খেদ আছে কষ্ট আছে, সব থেকে বেশী আছে গ্লানিকর অপবাদ। কেউ বিষ খেয়ে মরলেই সন্দেহ করে, জল্পনা-কল্পনা করে যে নিশ্চয় লোকটা কারুর কাছে মর্মান্তিকভাবে আহত হয়েছে, অপমানিত হয়েছে; অথবা নিশ্চয় এমন কিছু করেছে, যার জন্য সারা সমাজ এবং গভর্নমেন্ট তার বিরোধী হয়ে তাকে সাজা দেবে। সেই সব গ্লানি থেকে এড়াবার জন্য বিষ খেয়েছে।
তার থেকে মদ খেয়ে মরা ভাল। মদ খেয়ে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে এক ধরনের পাগল উল্লাস আছে, যা বিস্মিত করে দেয় সাধারণ মানুষের ঘৃণাকে, হতবাক করে দেয় কটু অপমানকর বাক্যকে
মোট কথা কীর্তিহাটে গিয়ে রায়বংশের পূর্ণ পরিচয় জেনে এবং পরিণাম দেখে পরিত্রাণ পাবার জন্য এদেশ থেকে পালিয়েছিলাম ইংল্যান্ড। কিন্তু সেখানে গিয়েও পেলাম না, রায়বংশের সম্পদলক্ষ্মী হারা রে-কে কলঙ্কের বোঝা সমেত ইংল্যান্ডে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিয়েছে। হারা রে আজ একা নয়, ওই মেয়েটি তার কে তা জানিনে, তাকে নিয়ে নির্লজ্জ ভাবে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে এবং ব্যাধির বীজ ছড়িয়ে দিচ্ছে।
সেখান থেকে পালিয়ে এসে এবার আমি ওই ধারাতেই বাঁচতে চাচ্ছি। যে কটা দিন বাঁচব, সে কটা দিন ওই ট্রাডিশন রেখে বাঁচাই ভাল।
পুরাণে ইন্দ্রপতনের কথা আছে।
রায়বংশের ছেলে মাত্রেই ইন্দ্র। তারা পড়লে যদি ইন্দ্রপতনের মহিমা দুনিয়াকে চমকে না দেয় তো মরেও যে শান্তি পাব না। এবং সে মৃত্যুতে যে চরম লজ্জা।
ইন্দ্রেরা বিলাসের ব্যভিচারের জন্য চিরকাল মুনিঋষির অভিশাপ মাথায় নিয়েছে।
বম্বে থেকে পনেরো দিন পর মন ঠিক করে যাত্রা শুরু করলাম। কিন্তু মিস মালহোত্রা বাধা দিলেন। না, মাই সন, এ তুমি করো না।
বললাম- না, এ ছাড়া আমার আর পথ নেই।
—কিন্তু এ পথ তো তোমার নয়! হলে তুমি হারা রে’র ভয়ে পালিয়ে আসতে না। হারা রে মেয়েদের কাছে ডেঞ্জারাস, হয়তো যারা তাকে জানে না, চেনে না, তাদের কাছে ভয়ঙ্কর কিন্তু তোমার কি ভয় ছিল তার কাছে? কিছু না। ইংল্যান্ডে অনায়াসে তাকে এ্যাভরেড করে আপন সুখের পথে চলতে পারতে। চল ফিরে চল, আমি তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যাব। আমার তোমাদের কীর্তিহাট দেখা হয়ে যাবে। তোমার বাবা আমার কাছে তোমাদের কীর্তিহাটের গল্প করতেন। কীর্তিহাট আমার কাছে ড্রীমল্যান্ড হয়ে আছে আজও পর্যন্ত। একটা মহলের কথা বলতেন “বিবিমহল’। ওয়ান্ডারফুল নাম। জাস্ট লাইক দি মুঘলস রঙমহল। চল।
কিন্তু তা আমি শুনি নি। বলেছিলাম, আমাকে তুমি মাফ কর। আমি স্থির করে ফেলেছি। এবং আই ডিফার উইথ ইউ, এই-ই আমার পথ। একমাত্র পথ। জমিদারের ছেলে আমি, আমাকে জমিদারের ছেলের মতই বাঁচতে হবে, যদ্দিন বাঁচব এবং মরতে হলেও জমিদারের ছেলের মত মরতে হবে এবং তাই মরব।
—কিন্তু গৌতম বুদ্ধ কি রাজার ছেলে ছিলেন না? তিনি কি রাজ্য ছেড়ে, সুন্দরী স্ত্রীকে ছেড়ে।
আমি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে বলেছিলাম- না, ওই একটা-দুটো ইতিহাসের নাম আমার কাছে অনুগ্রহ করে করো না। বুদ্ধ গৌতম একটা, হয়তো বা ইতিহাসে নাম ওঠে নি এমন সন্ন্যেসী হয়ে যাওয়া রাজা-জমিদারের ছেলে আরও একশো-দুশোও ছিল বা আছে। কিন্তু ওদের উল্টো মানুষের সংখ্যা কোটি দরুনে। আড়াই হাজার বছরে অনেক কোটি। প্লিজ লিভ মি। তুমি তোমার পথে যাও। আমার পথ আমি বেছে নিয়েছি।
পরের দিনই আমি মিস মালহোত্রাকে এড়াবার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। অজন্তা গুহা দেখব এবং সেখান থেকে হায়দ্রাবাদ।
নিজামের হায়দ্রাবাদ।
হায়দ্রাবাদ নিজাম হারেমে ক্ষুধিত পাষাণের সুন্দরীরা জীবন্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। হায়দ্রাবাদের চৌক-বাজারে রূপের হাটের জৌলুসে প্রদীপ আপনি জ্বলে ওঠে; সেখানকার গান-বাজনা-নাচের আসরে সেতারের তার আর্তনাদ করে ছিঁড়ে যায় না, তবলার বোলে ভুল হয় না, গানের তাল কাটে না।
১৯৪০ সাল সুলতা। আমার বয়স তখন তিরিশ। বিলেতে এক বছর থেকে ফিরেছি। আমার নিজের রূপের জলুস তখন কম ছিল না। বম্বেতে নতুন করে সব সরঞ্জাম কিনে নিলাম। কল্পনা ছিল সারাজীবনের সরঞ্জাম যোগাড় করে নিচ্ছি।
রঙ, তুলি, ইজেল ক্যানভাস কিনলাম নতুন করে। শুনে হয়তো তোমার মনে হচ্ছে যে, অজন্তায় গিয়ে পৃথিবীবিখ্যাত ফ্রেস্কোগুলোর নকল করব; কিন্তু না। ওসব তো অনেকে করেছেন। স্বয়ং নন্দলাল বসু করেছেন, অসিত হালদার মশাই করেছেন, আরও অনেকে করেছেন। আমি ওর জন্য এসব সরঞ্জাম কিনি নি। ওসব আমি কিনেছিলাম, অপরূপ রূপসী অবশ্যই দেখতে পাব, তাদের ছবি আঁকব বলে।
আর কিনেছিলাম একটা দামী বেহালা, আর বাঁশের বাঁশী। বাজাব। গান-বাজনার আসরে তেমন গান শুনলে আমি বাজিয়ে সঙ্গত করব।
সুরেশ্বর বললে-সংসারে মানুষের জীবনে কার্যকারণেই হোক বা ভবিতব্যের বিধানেই হোক, যা ঘটবার তার বিপরীত কিচ্ছু ঘটানো যায় না। সংকল্প করেও তা ঘটাতে পারে না মানুষ। দু-এক ক্ষেত্রে অসাধারণ শক্তিশালী মানুষ সংকল্প করে ঘটনার গতিরোধ করে বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার দাম দাঁড়ায় যৎসামান্য।
আমি সংকল্প করেছিলাম—নিজেকে আমি ভাসিয়ে দেব বা রায়বংশের বড় বড় পুরুষগুলির জীবন যে খাতে প্রবল স্রোতে বয়ে গেছে সেই খাতে সেই স্রোতে গা ভাসিয়ে দেব; কোন খালে-বিলে বা পঙ্কপল্বলের মধ্যে হারিয়ে যাব।
হারা রায় এবং শম্পা রায়ের বিবরণ আমাকে উন্মাদ করে তুলেছিল এবং মিথ্যে কথা বলব না, জীবনে তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করেও যে তীব্র কামনায় উন্মাদের মত রাবণ সীতাকে হরণ করেছে, শিব মোহিনীর পিছনে ত্রিভুবন ছুটেছে সে কামনা আমি অনুভব করি নি। ইংল্যান্ডে শম্পা রায়কে দেখে আমার জীবনকামনা ভীত হল—আমাকে বললে, “ভীত হও তুমি। নত হও তুমি।”
বম্বেতে এসে কয়েক দিন মদ খেলাম, আর রায়বংশের হিসেবনিকেশ করলাম। এবং নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বললাম, তুমিই বা এমন পঙ্গুর মত বা ওয়ারেন্টের আসামীর মত এমন ভাবে লুকিয়ে বেড়াচ্ছ কেন? দোহাই তোমার, ছিঁচকে চোর তুমি হয়ো না, দুর্ধর্ষ গুন্ডা হও। পিতৃপুরুষের পথ ছাড়া তোমার পথ নেই, আর সে পথে পায়ে হেঁটে কোন কিছুর আড়াল দিয়ে চলবার উপায় নেই, ওপথে রাবণের পিঠে সওয়ার হয়ে ছুটতে হবে অথবা রথে চড়ে ছুটতে হবে।—তাই ছোটো।
রঙ-তুলি বেহালা বাঁশী কিনে বম্বে থেকে এলাম হায়দ্রাবাদ। জাঁকজমক করে হায়দ্রাবাদের বড় হোটেলে উঠলাম। হোটেলেই ভালমন্দ সকল পথের পথিকদের পথ দেখাবার জন্যে পথের দিশারী আছে। তাদের বকশিশ দিলাম। সেলাম নিলাম। সব আয়োজনই করলাম কিন্তু ভেসে যেতে পারলাম না, রায়বংশের জীবনস্রোত আমাকে ওই খাতে ভাসিয়ে নিয়ে গেল না—আরও একটা খাত বেয়ে গিয়েছিল, কীর্তিনাশা পদ্মার প্রবল স্রোতকে পাশে রেখে ভাগীরথীর ধারার মতো সেই খাতে আমাকে টেনে নিয়ে গেল।
ভাগীরথী আর কীর্তিনাশা নাম দুটো ব্যবহার করছি বলে ভেবো না নিজেকে ভগীরথের সঙ্গে তুলনা করছি, রায়বংশের মুক্তিদাতা উত্তমপুরুষ বানাচ্ছি নিজেকে। না, তা বানাচ্ছি না। ভাগীরথীর বদলে ‘হুগলী নদী’ বলব বা বলছি তাহলে।
আমি পারলাম না ভেসে যেতে; ওই উদ্দাম জীবনস্রোত যেন ব্যঙ্গ করে ঢেউয়ের ধাক্কায় ক্ষীণস্রোতা পাশের ছোট শাখাটার মুখের দিকেই ঠেলে দিলে।
একটু থামলে সুরেশ্বর, তারপর বললে—তা ছাড়া সুলতা, তুমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি এবং রাজনীতি বিজ্ঞানের অধ্যাপিকা, তুমি একথা নিশ্চয় মানো যে, মানুষের জীবনের গতি এবং তার পরিণতি শুধু তার ব্যক্তিগত এবং বংশগত ভাগ্যলিপি বা কর্মচক্রেই চলে না; কালের একটা হাওয়া আছে মহিমা আছে। সেটা চিরকাল আছে। ভাগীরথী যেদিন এসেছিলেন এবং সমুদ্রে মিশেছিলেন, সেদিন শুধু অভিশপ্ত সগর-সন্তানেরাই উদ্ধার হয় নি—আরও বহু বহু হয়তো কোটি কোটি পতিত আত্মা উদ্ধার পেয়ে গিয়েছিল পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার জলের মহিমায়। কালের মহিমা বা হাওয়ায় সাহায্য করেছিল।
কালটা ১৯৪০ সাল, মার্চ মাস। ইয়োরোপে পোল্যান্ডের করিডোর নিয়ে শুরু যে যুদ্ধ তা ধীরে ধীরে কমাসে গোটা পোল্যান্ডের উপর ভারী রোলারের মত গড়িয়ে চলে এবার দ্রুতবেগে চলতে শুরু করেছে। সোভিয়েত রাশিয়া অর্ধেক পোল্যান্ডের ভাগ নিয়ে ওদিকে ফিনল্যান্ড নিয়েছে। এদিকে জার্মানী নরওয়ে দখল করে ফ্রান্সে ঢুকে, ব্লিৎসক্রিগ চালিয়ে ফরাসী এবং ইংরেজ বাহিনীকে ঠেলে নিয়ে চলেছে ইংলিশ চ্যানেলের দিকে। ব্রেনার গিরিবর্তে হিটলার মুসোলিনীর সঙ্গে দেখা করেছেন।
সারা ভারতবর্ষ থমথম করছে। প্রতীক্ষা করছে গান্ধীজী এবং কংগ্রেস কোন্ নির্দেশ দেবেন মানুষকে। অন্যদিকে ভারতবর্ষ প্রতীক্ষা করছে সুভাষচন্দ্র কি বলবেন! কংগ্রেসের মধ্যে জয়প্রকাশ নারায়ণ, অশোক মেহতারা কি বলবেন! কি নির্দেশ আসবে! যে নির্দেশ যিনি দিন, সে নির্দেশ মারবার এবং মরবার হুকুমের চেয়ে কম হলে বুক ভরবে না কারুর। সে সামান্য নিরক্ষর জনেরও না।
সুলতা, এমন সময় যখন আসে তখন এমন একটা হাওয়া বয়—যেটা বৈশাখী দুপুরের হাওয়ার মত আগুনকে দ্বিগুণ করে জ্বালিয়ে তোলে। সে সময়ে সর্বনাশের নেশা লাগে বটে কিন্তু সুরা আর নারী নিয়ে ব্যভিচারের নেশা নয়। সে নেশা ঠিক তার উল্টো নেশা।
হায়দ্রাবাদের একটা ঘটনা বলি। ঘটনাটা শিলালিপির মত অক্ষয় হয়ে আছে বুকে। সুভাষচন্দ্ৰ ১৯৪০ সালের ১৮ই মার্চ রামগড়ে আপোসবিরোধী সম্মেলনে যে বক্তৃতা দিয়েছেন, সেই বক্তৃতার কাগজ মদের গ্লাস হাতে করে পাশে সরিয়ে দিয়েছি কিন্তু আশ্চর্য, নেশা জমে নি এবং কখন যে গ্লাসটা নামিয়ে কাগজখানা টেনে নিয়েছি তা খেয়াল করি নি।
ঘণ্টা দুয়েক বসেছিলাম এইভাবে।
কালটাই ছিল সুরা ও নারীর নেশা ছাড়বার ছুটবার কাল; নেশা করব বলে সংকল্প করলেও সে সংকল্প রাখতে পারি নি। তাছাড়া আরও এক ধরনের মানসিক বিভ্রান্তি ঘটত, সেটাও আমার এই জবানবন্দীর মধ্যে বলে যাই।
সেটা শুধু আমার জীবনের সত্যই নয়, গোটা রায়-বংশেরই জীবনসত্য সেটা। মদের নেশার ঘোর বাড়লেই চোখে কেমন দৃষ্টিবিভ্রম ঘটত।
সেদিন হায়দ্রাবাদের হোটেলে নিজেকে সবে প্রস্তুত করে নিচ্ছি; প্রস্তুত অর্থে সুলতা মদের নেশাটাকে বেশ প্রখর করে তুলে মনে মনে ভাবছি রায়বংশের ধুরন্ধর রায়দের কথা; কুড়ারাম রায় ভটচাজের বৈষ্ণবীর কথা, সোমেশ্বরের সেই মনোহারিণী ব্রাত্যনারীর কথা, শ্যামাকান্তকে বর্ষার কাঁসাইয়ে ফেলে দিয়ে যাকে তিনি নিজে গ্রহণ করেছিলেন, বিকৃতমস্তিষ্কা কামার্তা মেয়েটা এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরত। বিশদ বিবরণ থাক, সবই জান, মোট কথা রায়বংশের রুচি ও রীতিগুলোকে স্মরণ করে নিজেও ওই ছাঁচে নিজেকে ফেলব বলে তৈরী হচ্ছি—এমন সময় হোটেলের দালাল এসে সেলাম জানিয়ে দাঁড়াল। বললাম —কি খবর?
সে দুটি বাঈকে নিয়ে এসেছে; অর্থাৎ দেখাতে এনেছে। এরাই নাকি হায়দ্রাবাদের রূপের হাটের সব থেকে সেরা রূপসী পসারিনী, এবং রূপের হাটে রূপ ছাড়া যে গুণের প্রয়োজন সেই গুণের অধিকারিণী—নাচা-গানায় অদ্বিতীয়া; দালাল বললে—ই দোনোকে জড়ী বাঈ তামাম হায়দ্রাবাদমে নেহি মিলেগী। বললে-ওরা বাইরে বসে আছে, ডাকব ভিতরে?
কেমন সংকোচ বোধ করলাম। মোট কথা, ব্রজদার শেফালির পাড়ায় যে সংকোচ অনুভব করেছিলাম, সেই সংকোচ আড়ষ্ট করলে আমাকে। ব্রজদার শেফালির পাড়াতে তবু তো দয়া করুণা উদারতার বাস্কেট মাথায় করে দয়া চাই করুণা চাই হাঁক দিয়ে আড়ষ্টতা কাটিয়েছিলাম, ব্রাভাডো ছিল, এখানে তার কিছুই পেলাম না এবং নার্ভাস হয়ে বললাম—“না—ডাকতে হবে না।”
—তা হলে?
—বারান্দায় বসে আছে বলছ?
—হাঁ হুজুর, যেখানে লোকজন এসে বসে।
আমি বললাম, আমি বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে ওদের দেখে আসছি। বুঝেছ?
সে বললে–আপনি কেন শরম করছেন হুজুর। এখানকার হালই এমনই। ওরা ডাকলে হোটেলে আসে। নাচা-গানা এখানে ভাল হয় না কিন্তু —।
সুরেশ্বর স্তব্ধ হয়ে গেল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, বাকীটা তুমি বুঝতে পারছ সে কি বলেছিল! বোধ করি হোটেল-জগৎটাতেই এ রীতি—সেই অন্ধকার কাল থেকে একাল পর্যন্ত সমগৌরবে এবং কালোপযোগী পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয়ে খোলস বদলে বদলে সমান শ্রদ্ধায় চলে আসছে।
ট্রেড-জগৎ বড় বিচিত্র জগৎ; ট্রেডের মধ্যে অনেস্টি আছে এবং অনেস্টিই হল সব থেকে বড় ক্যাপিট্যাল কিন্তু শুচিবাই ওখানে অচল। শুচিবাই চলবে না। অনেস্টির জন্য হোটেলে মেয়েদের আনাগোনা করতে দিতে হয়। না দিয়ে উপায় নেই।
তত্ত্ব আলোচনা থাক। যা ঘটেছিল বলি—আমি তাদের দেখে এলাম। বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে রেলিংয়ে ভর দিয়ে তাদের দিকে ফিরে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মেয়ে দুটি পরস্পরকে ইশারা করে হাসাহাসি করতে লাগল। এবং হাস্যের সঙ্গে কিছুটা লাস্য আপনি তাদের সারা অঙ্গ থেকে ঝরে পড়ল। ভাল লাগল আমার।
মুসলমানী বাইজী। একজন ফিরোজা, সে তরুণী এবং অন্যজনের নাম জুলেখা, সে পরিপূর্ণ যুবতী। রবীন্দ্রনাথের ‘দে লো সখি দে, পরাইয়ে গলে সাধের বকুল ফুলহার’ গানের গায়িকার মত যুবতী। তার মাথার মিহি ওড়নাখানা সত্যই বার বার মাথা থেকে খসে পড়ছিল। বার বার সে তুলে নিচ্ছিল লীলাচ্ছলে। হঠাৎ কোথায় কোন্ ঘর থেকে কলিংবেল বেজে উঠে আমাকে চমকে দিলে; আমি আত্মস্থ হয়ে ঘরে ফিরে এলাম; দালালটাও আমার পিছন পিছন এল এবং আমার সোফার পাশে দাঁড়িয়ে বললে—আব ফরমাইয়ে বাবুসাব। হুকুম তো হো যায় আপকা। আমি মদের গ্লাস যেটা ফেলে গিছলাম, সেটা তুলে নিয়ে চুমুক দিয়ে বললাম- ঠিক হ্যায়। সন্ধ্যার পর যাব, মহফিল হবে।—
–বলুন কাকে চাই!
ভেবে ঠিক করতে পারি নি, রূপ চাই না যৌবন চাই, নাচ চাই না গান চাই-এর তো এক মুহূর্তে মীমাংসা হয় না। যারা মীমাংসা করে নিতে পারে, তারা রূপও চায় না যৌবনও চায় না, গানও চায় না, নাচও চায় না, চায় একটি নারীদেহ। তারাই সংসারে বেশী। সুলতা, আমি বোধ হয় তা নই। রায়বংশে জন্মে যে কেমন করে এমন হয়েছি আমি একথা ভেবে পাইনে। কালের কথা বলেছি, বাবার জীবনের চরমতম ট্র্যাজেডির কথা জান, মায়ের চোখের জল দেখেছি, ধনেশ্বরকাকার দৈত্যের মত ছেলেটার পরিণাম —তাও আমার চোখের সামনে ঘটল-হয়তো সেই জন্যে এমন আমি। তার উপর আমি আর্টিস্ট—শুধু দেহ নিয়ে আমার মন ভরে না, আমি বোধ হয় রূপ যৌবন গুণ অর্থাৎ নাচগান বিচার করতে চাই। তাই বলেছিলাম—দুজনেই থাকবে মহফিলে। একজন গাইবে, একজন নাচবে।
লোকটা ‘সাবাস, সাবাস’ করে উঠেছিল এবং বড়রকম মক্কেল মনে করে বার বার তসলীম জানিয়েছিল। ফলে রাত্রে ওদের আস্তানায় যে মহফিলের আসর বসেছিল—তাতে জলুসের একটু বাড়াবাড়ি করেছিল। সেটা আমাকে কায়দা করবার জন্য বা গাঁথবার জন্য।
আমার খারাপ লাগে নি।
জীবনে রাজাগিরি, বাদশাগিরি, নেতাগিরি যাই বল না কেন সবই বলতে গেলে ‘আবুহোসেনি’ ব্যাপার।
আবুহোসেন নিশ্চয় জান—আরব্য উপন্যাসের গল্প, হারুণ অল রশিদের হুকুমে মসরুর দেউলে-পড়া উদার বণিকপুত্রকে রাত্রির মত বাদশা বানিয়ে দিয়েছিল। গিরিশবাবুর একখানা নাটক আছে এই উপাখ্যান নিয়ে। আবু হোসেন সেজেই বসেছিলাম খুশীর সঙ্গে।
গ্রীষ্মকাল। আরব সাগর বা বঙ্গোপসাগরের জলো বাতাসের ঝলক তখনও নিজাম রাজ্যে এসে পৌঁছয় নি; গরমের মেজাজ তখন চড়া কিন্তু মুসলমানী আমীরিয়ানার ব্যবস্থায় আরামের আয়োজনের ঘাটতি ছিল না। সে তোমার গোলাপজলের ঝাঁঝরিওয়ালা পিচকারি, গোলাপপাশ, বেলকুঁড়ির মালা, সুবাসিত পান, আতর, ঠাণ্ডাই শরবৎ নিয়ে জাফরী-কাটা আলসে ঘেরা খোলা ছাদের উপর আসর বসেছিল একটি খণ্ড স্বপ্নালোকের মত। তার সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের দান ইলেকট্রিক লাইট ফ্যান।
বরফ দিয়ে ঠান্ডা করা বীয়ার এবং দামী হুইস্কি। সারেঙ্গীদার তবলচীরা বসেছে গোঁফে তা দিয়ে, গলায় বেলকুঁড়ির মালা দুলিয়ে।
মেয়ে দুটি সেজেগুজে এসে বসল, সঙ্গে সঙ্গে দুটো বড় স্ট্যান্ডিং লাইটের সুইচ অন করে দিলে। আমি অবাক বিস্ময়ে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এত রূপ! বা রূপের এত ঐশ্বর্য! রূপকে এমন অপরূপ করা যায়, যা পুরুষের মনকে মুহূর্তে লালসায় কামনায় স্থানকালপাত্র সব ভুলিয়ে দিতে পারে!
সঙ্গতের যন্ত্রের সুর বাঁধা হচ্ছিল। আমি তাকিয়েছিলাম ওই ওদের দিকে। ইংল্যান্ডে ঠিক এই ধরনের পরিবেশ হয় নি। এমন করে ওরা সজ্জা করে অপরূপ হয়ে মন ভুলোতে পারে না। অবশ্য হোটেলে নাচ হয়, সেখানে মেয়েরা সেজে আসে। তার মধ্যে তনুদেহের অনাবৃত বিজ্ঞাপন পুরুষকে চঞ্চল করে তোলে। বুকের মধ্যে রক্তধারা বাঁধভাঙা নদীস্রোতের মত ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু তার থেকেও ভারতীয় প্রথা যেন বেশী মোহময়ী।
যুবতী মেয়েটি একেবারে গৃহের গৃহিণীর মতই অতিথিসৎকারে তৎপরা হয়ে উঠল। এগিয়ে এসে প্রথম পানের খিলি এগিয়ে দিলে, তারপর বোতল থেকে ঢেলে গ্লাস পূর্ণ করে সোডা মিশিয়ে একটি পরাতে করে আমার সামনে ধরে দিয়ে উর্দুতে বললে—খেতে হুকুম হোক রাজাবাবু!
আমি গ্লাসটি নিয়ে বললাম- তোমার নাম জুলেখা!
—আমি হুজুরের বাঁদী।
—তোমরা খাবে না?
—হুকুম হলে খাব। কিন্তু হুজুরকে নাচা-গানায় খুশী করতে হবে।
গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে তাকে দেখছিলাম। গ্লাসটা শেষ করে নামিয়ে দিলাম—তখন গান সবে শুরু হয়েছে। চোখ বুজে শুনতে লাগলাম। ভাল গায় মেয়েটি। সত্যিকারের ভাল গায়।
এরই মধ্যে ঠং করে শব্দ উঠল, সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টি গলায় ডাক শুনলাম -বাবুসাব!
চোখ মেলে দেখলাম, তরুণী মেয়েটি গ্লাস ভরে নিয়ে সামনে ধরেছে। আমি হেসে হাত বাড়িয়ে গ্লাসটি নিলাম। নেবার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল বীরেশ্বর রায়ের কথা। সোফিয়াকে নিয়ে বীরেশ্বর রায় এমনি ভাবেই জানবাজারের বাড়ীতে আসর পাততেন।
মনের মধ্যে যেন একটা আমীরী আমেজ অনুভব করছিলাম। পকেটে হাত দিয়ে আমার টাকার থলিটা নাড়লাম—বকশিশ দেব। গ্লাসটা চুমুক দিয়ে শেষ করে নামিয়ে দিয়ে বললাম—আবার ঢালো!
মেয়েটি ঢালতে লাগল। আমি একটা সিগারেট ধরালাম। মেয়েটি গ্লাসটি আমার হাতে ধরিয়ে দিতেই আমি বললাম, এটা তুমি খাও।
মেয়েটি ফিক করে হাসলে।
তারপর গ্লাসটা হাতে নিয়ে ঠোঁটে ঠেকিয়ে নামিয়ে রেখে আমার সিগারেটের টিন থেকে সিগারেট বের করে ধরিয়ে ডান হাতখানা আমার সামনে পেতে বললে, টাকা দাও বাবুজী!
আমি একটু বিস্মিত হলাম। চলে যেতে চায় নাকি?
মেয়েটা বুঝতে পারলে আমার মনের প্রশ্ন। সে বললে—মুজরায়—গানাবাজানার -নাচনার আসরে দারু আমরা খাইনে বাবুসাহেব, দারু খাই মহব্বতির আসরে। আমার সঙ্গে মহব্বতি করতে হলে সে অনেক টাকার কারবার বাবুজী। তবে বকশিশ করলে আমরা কিছু কিছু দারু খাই। প্রথমেই তো কিছু বকশিশ করো।
আমি স্থিরদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।
হাতখানা পেতে মেয়েটা সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে বললে, আমার পাওনা বকশিশ দাও বাবুজী!
মদের নেশার মধ্যে আমি চমকে উঠলাম। আমার মনে পড়ে গেল, আর একজনের কথা, ঠিক এইভাবে সিগারেট টানতে টানতে, আমার সিগারেটের টিন থেকেই সেও সিগারেট নিয়েছিল, বলেছিল—give me my dues.
লরা নাইট ওরফে শম্পা রায়। যাকে দেখে মনে হয়েছিল যেন রায়বংশের মুখের গড়নের সঙ্গে ছাঁচের সঙ্গে একটা মিল আছে। সেও বলেছিল—give me my dues.
ফিরোজা—ফিরোজা মেয়েটার নাম, সে তখনও বলছিল- দাও বাবুজী, আমার পাওনা বকশিশ দাও!
পকেট থেকে একখানা দশ টাকার নোট বের করে তাকে দিয়ে নিজেই টেনে নিয়েছিলাম হুইস্কির বোতলটা এবং একটা নতুন গ্লাস।
পর পর বোধ হয় দু’তিন গ্লাস মদ খেয়েছিলাম। মনের মধ্যে কি যেন একটা আতঙ্কের মতো পাক খাচ্ছিল—যেন কত উদ্বেগ বুকে জমা হয়ে মুহূর্তে মুহূর্তে ভারী হয়ে উঠছিল। মনে পড়ছিল রায়বংশের ইতিহাস। যে ইতিহাস আমি সেটেলমেন্টের সময়ে গবেষকের মত পড়েছি—জেনেছি। কুড়ারাম ভটচাজ থেকে যোগেশ্বর রায়—আমার বাবা পর্যন্ত সকলকে মনে পড়েছে, মেজকাকু শিবেশ্বর রায় এবং তার ছেলে ব্রজেশ্বর আর সেই দৈত্যটাকে মনে পড়েছে আর ভয় পেয়েছি। ক্রমাগত একটা প্রমত্ত উল্লাস নাচতে নাচতে দু হাতে ডাক দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছিল আর তার পিছনে পিছনে আসছিল একটা ভয়ঙ্কর ছায়া—সে আসছিল দু হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরতে।
এরই মধ্যে আমার মদের নেশার প্রভাবে আমার চোখে কি করে যে ওই তরুণী মেয়েটার চেহারা পাল্টে গেল তা আমি জানি না। কিন্তু বিশ্বাস কর—গেল। একেবারে পাল্টে গেল। ফিরোজার পোশাক ছিল সেদিন চুড়িদার পায়জামার উপর পেশোয়াজ কাঁচুলি ওড়না, নাকে গয়না, কানে গয়না, কপালে টিকলির ধুকধুকি, কৃষকষে কালো তৈলমসৃণ চুলে জরি জড়ানো লম্বা বেণী; গলায় জড়োয়ার কণ্ঠী। হাতে কঙ্কণ চুড়ি। কিন্তু আমার মনে হল ফিরোজা নয়, এ সেই শম্পা রয়, অবিকল শম্পা রয়-সে কোন থিয়েটারের গ্রীন রুম থেকে পাকা মেকআপ-ম্যানের হাতে হায়দ্রাবাদের নাচওয়ালী সেজে এসেছে।
বার বার মুখের দিকে তাকালাম। কিছুতেই ফিরোজাকে আবিষ্কার করতে পারলাম না। তার এতটুকু সন্ধান মিলল না। শম্পা রয়। অবিকল রায়বাড়ির ছাঁচের মুখ।
বার বার অস্বীকার করলাম- না, নয় নয় নয়।
স্থিরদৃষ্টিতে মেয়েটার দিকে তাকিয়েই মনের ভ্রমের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলাম—অস্বীকার করছিলাম, না—নয় নয় নয়।
মেয়েটা তখন ওই যুবতী গাইয়ে মেয়ে জুলেখার সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে কথা বলছিল।
আমি ডাকলাম—শোন!
সে মুখ ফেরালে- ফরমাইয়ে।
এবার মনে হল, না-শম্পা নয়—সে মেয়েটা মেমসাহেব। এ এ-দেশের মেয়ে, কিন্তু ফিরোজা নয়। মুখে রায়বাড়ীর ছেলেমেয়ের মুখের ছাপ রয়েছে। অবিকল রয়েছে। এতটুকু ভুল হয় নি আমার।
মনে হল—অনেকটা অর্চনার মত দেখতে।
হ্যাঁ, অর্চনার মত।
আমি চোখ বন্ধ করে অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে বললাম—আঃ!
জুলেখা এসে আমার হাত ধরে বলেছিল—বাবুজী, বাবুজী, বাবুজী!
আমি চমকে উঠে সাপ দেখে যেমন সরে যায় তেমনি করে সরে গেলাম। সকলে চমকে উঠল। গানের আসর ভেঙে গেল।
—কি হল—বাবুজী—বাবুজী!
–কুছ না। পানি। এক গিলাস পানি
ঠান্ডা জল নিয়ে এগিয়ে এল জুলেখা যুবতী মেয়েটি। আশ্চর্য, জুলেখার মুখের চেহারাও যেন পাল্টে গেছে!
তার মুখেও দেখেছিলাম যেন রায়বাড়ীর কোন বধূর মুখ। ছবিতে দেখা মুখ।
আবার মনে হয়েছিল, না। রায়বাড়ীর কর্তাদের কোন অনুগৃহীতার মুখ। ঝপ করে ভেসে উঠেছিল মিস মালহোত্রার মুখ। না। পরমুহূর্তে মনে হয়েছিল—না, তার মত নয়। তবে কারুর মত বটে। তাকে হয়তো চিনিনে। হয়তো সোফিয়া।
আমি আতঙ্কিতের মত উঠে দাঁড়িয়ে দালালটাকে বলেছিলাম- আমার শরীর খুব খারাপ মালুম হচ্ছে, ট্যাক্সি ডাক। আমি হোটেলে ফিরব। দুখানা একশো টাকার নোট দিয়ে বলেছিলাম—জলদি করো। জলদি।
জুলেখা এসে আমার হাত ধরে বলেছিল—বাবুজী, বাবুজী, বাবুজী!
আমি ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠেছিলাম এবং বলেছিলাম—ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও, ছোড় দো—মুঝে ছোড় দো। মুঝে ছোড় দো!
শ্যামাকান্তের আর্তনাদের প্রতিধ্বনি বোধ হয় আমার কথার মধ্যে ফুটে উঠেছিল সুলতা।
আমি সেই যে হায়দ্রাবাদের জুলেখা বাঈয়ের বাড়ী থেকে পালিয়ে এলাম, তারপর আর জীবনে নারীর জীবন-যৌবন-নীরে অবগাহন করতে ছুটে যাই নি। একটা ভয়, হ্যাঁ, একটা ভয় যেন আমার পা টেনে ধরত। কত সুন্দরী মেয়ে—কেউ আমার রূপে, কেউ আমার শিল্পী-খ্যাতির আকর্ষণে, কেউ আমার অর্থের জন্যে আমাকে আকর্ষণ করেছে, আমিও আকর্ষণ অনুভব করেছি, কিন্তু তবু এগুতে পারি নি। কেমন যেন ভয় পেয়ে এক পা এগিয়ে দু পা পিছিয়ে এসেছি। মনে মনে এ নিয়ে অনেক ভেবেছি-কেন? এমন হয় কেন? নারীর জীবনস্রোত যৌবনের রূপের খাতে অনন্তকাল বইছে এবং পুরুষেরা দলে দলে ছুটে এসে সেই আদিকাল থেকে এই স্রোতে ঝাঁপ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। সেখানে আমি তার তীরের ঘাটে এসে ভয় পেয়ে জলাতঙ্ক রোগীর মত ফিরে যাচ্ছি কেন?
কত রকম মনে হয়েছে। সে-সব কথা থাক। এক-একবার ভেবেছি—কোন মনের ডাক্তারের কাছে যাই। কিন্তু যাই নি। কি হবে গিয়ে, তারা যা বলবে সে আমার অজানা ছিল না।
আমি তো বুঝতেই পারছি—এ আমার ভ্রম। আমার বাবার জীবন, মায়ের মুখ, মেজদাদু শিবেশ্বর রায়ের পরিণাম—তাঁর দৈত্যের মত পৌত্রটার পরিণতি, চোখে দেখে এবং রায়বাড়ীর দপ্তর ঘেঁটে এ-বংশের নারীজীবন নিয়ে একটা অস্বাভাবিক আসক্তির ইতিহাস পড়ে আমার মনের অবস্থা এমনি হয়েছে। ব্যাধি আমার ওইটেই। রায়বংশের ইতিহাসকে আমাকে ভুলতে হবে। মনের ডাক্তার আমাকে এই কথাই বলবেন তা আমি জানতাম। বলবেন—ভুলে যান। ওসব ভুলে যান। পৃথিবীতে এইটেই চিরকালের নর-নারীর জীবনের ধারা। আপনাদের বংশের প্রতাপ ছিল, প্রতিপত্তি ছিল, অর্থ ছিল, সম্পত্তি ছিল, স্বাভাবিক ভাবে আপনাদের বংশের পূর্বপুরুষেরা weaker sex-কে টাকা দিয়ে কিনেছেন, প্রতাপ-প্রতিপত্তিতে কেড়ে এনেছেন—কেউবা হয়তো পুরানোকালের বিশ্বাসবশে ধর্মসাধনা করে Spiritual Power দিয়ে মেয়েদের আয়ত্ত করতে চেয়েছেন। অবশ্য এই পাওয়ার কি, তা তাঁরাই জানেন। যখন যেমন যুগ। ফরগেট অল দোজ থিংস। এ-কালে যেমন যুগ সেইভাবে কোন নারীকে জীবনে পাবার চেষ্টা করুন এবং বিশ্বাস করুন, আপনি শুধু আপনার নিজের জন্যে রেসপনসিল, অন্য কারুর জন্যে নয়; এমন কি কাল কি করেছেন, তার জন্যে অনুশোচনা না করে বিগিন লাইফ উইথ এ ক্লীন স্লেট ফ্রম টু ডে এবং তার মধ্যেই দেখবেন আপনি পাপীও নন পুণ্যাত্মাও নন, আপনি গুড সিটিজেন। সহজ মানুষ। এর সবই আমি মানি—এ আমারই কথা সুলতা, কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই সুলতা, তা আমি পারি নি। কিছুতেই পারি নি। এর জন্যে যে আমাকে যা বলবে আমি প্রতিবাদ করব না, মেনে নেব।
মনে কেমন একটা সংকল্প জাগল, রায়বাড়ীর অন্য শাখার স্রোত যতদিন চলে চলুক, যতদূর চলে চলুক, দেবেশ্বর রায়ের ছোটছেলে যোগেশ্বর রায়ের জীবন ধরে যে স্রোত এখন সুরেশ্বর রায়ের দেহের খাতে বেয়ে চলেছে, তাকে আমি শেষ করে দেব এবং রায়বাড়ীর সম্পত্তির শক্তিবলটাকেও নিঃশেষিত করে দেব। নানান রকম কল্পনা করতাম, কখনও কল্পনা করতাম গ্রামে গ্রামে কো-অপারেটিভ করে জমিদারীর মালিকানা তার হাতে দেব-কখনও ভাবতাম সরকারকেই ইস্তফা দিয়ে যাব। মেদিনীপুরে গভর্নমেন্টের খাস জমিদারী অনেক আছে, সেইমত ব্যবস্থা হবে। কখনও ভাবতাম বিক্রী করে দিয়ে সেই টাকায় একটা বড় কিছু করে দিয়ে যাব। যার থেকে রায়বংশের কোন শাখার কেউ যেন এতটুকু পাথেয় না পায়।
ভেবেছিলাম কোন একটা আশ্রমে চলে যাব। ১৯৪০-৪১ সাল। কালের দিক থেকে একটু বিলম্বিত হলেও, কালটায় আশ্রমবাসী হওয়ার একটা ঝোঁক তখনও বিগত হয় নি। কিন্তু তা-ও পারি নি; কারণ ঈশ্বর ধর্ম-ধ্যান-জপ এ আমার পক্ষে বিষম বস্তু ছিল। কীর্তিহাটে ঠাকুরবাড়ীতে যেতাম চরণোদক খেতাম না, মাথায় নিতাম, বাল্যভোগের প্রসাদ দু-চার দিন খেয়েছি, এ সবই সত্যি, মিষ্টি ফল আমিই কিনে দিতাম—খেতেও মিষ্ট লাগত, প্রণামও করেছি—তার মধ্যে ভক্তি কিংবা সত্যবোধ ছিল না সুলতা, যখনই ঠাকুরবাড়ী গেছি, যখনই ঠাকুরদের কথা ভেবেছি তখনই মনে হয়েছে, ওই কালী-ঠাকুরুণটির এবং রাধাসুন্দর-ঠাকুরটির আমি অন্নদাতা পিতা। ওরা একান্তভাবে আমার। তবে মুখে সেটা কোনদিন প্রকাশ করি নি। আমাদের দেশে তো ঠাকুরে-ঠাকুরে লড়াই হয়, এবং সে লড়াই তাঁরা করেন ওই পালক-পিতাদের হুকুমে। বিসর্জনের সময় কার প্রতিমা আগে যাবে এই নিয়ে বড় বড় খুন-জখম এবং স্বত্বের মকদ্দমার নজির পাবে হাইকোর্টে। ছোটতরফ বড়তরফের কালী-প্রতিমারা ছোটবাবু আর বড়বাবুর হুকুমে নদীর দিকে ছুটেছে; এ ওর পথ আগলেছে, ও এর পথ আগলেছে। লড়াই করতে গিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ে চুরমার হয়েছে। মুসলমানদের তাজিয়া নিয়ে এমন মামলা বছর বছর হয়। সুতরাং ধর্ম বা ধর্মের আখড়ার দিকে আমার আকর্ষণ কিছু ছিল না। ইদানীং অবশ্য অনেক ভোগী মডার্ন সন্ন্যাসীদের আশ্রম হয়েছে, যেখানে তপস্যা থেকে ভোগ বড়, কিন্তু তাদের প্রতিও আকর্ষণ ছিল না। আমি চেয়েছিলাম জীবনে মুক্তি। সে-মুক্তি কেমন করে কোন্ পথ ধরে আসবে জানি না, তবে চেয়েছিলাম তাই।
বিশ্লেষণ করে বলতে পার জমিদার বা ধনীপুত্রের আর এক ধরনের মনোবিলাস। আমি অস্বীকার করব না। অনেকটা তাই-ই বটে। সেকেন্ড ক্লাসে বার্থ রিজার্ভ করে দক্ষিণ থেকে শুরু করে উত্তরাবর্ত অভিমুখে মুক্তি খুঁজতে খুঁজতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ তাতে ছেদ পড়ল। সময়টা কালীপুজোর পর সম্ভবতঃ রাস-পূর্ণিমার আগের দিন-আমি ছিলাম তখন হরিদ্বারে। হরিদ্বার বড় ভাল লেগেছিল। ভাবছিলাম এই অঞ্চলেই শেষ জীবনটা কাটিয়ে দিলে কেমন হয়। হরিদ্বার থেকে হৃষিকেশ লছমনঝোলা পর্যন্ত অঞ্চলটির কোন একটি স্থানে একখানা ঘর বানিয়ে ছবি এঁকে জীবন কাটালে কেমন হয়? হঠাৎ অর্চনার চিঠি এল। কলকাতা থেকে অৰ্চনা লিখেছে—
সুরোদা,
বৃন্দাবন থেকে খবর দিয়েছে বড়ঠাকুমা, লিখেছেন এবার আমি যাব। লিখেছেন তোমাকেই, লিখেছেন—ভাই, কীর্তিহাটের বড়বাবু, আমার স্বামীর মৃত্যুর পর আমি রায়দের সঙ্গে বন্ধন কেটে চলে এসে বৃন্দাবনে আমার ভিক্ষে-শাশুড়ীর পাপের অন্নের পিশু গোবিন্দের নাম নিয়ে খেয়ে বেঁচে আছি। ছেলেরা খোঁজ করে নি। আমার বাপের লাখ টাকা ছিল, তা ছেলেরা ঘর ছেড়ে চলে এসেছি বলে নিজেরা নিয়েছে। তাতে ক্ষোভ ছিল না, খেদ ছিল না। তারা ভুলেছিল তাতেও মনে ভাটা পড়েছিল—হঠাৎ তুই বার-দুই এসে ঠাকুমা বলে ডেকে নতুন করে রায়বাড়ীর ছেঁড়া বাঁধনে গিঁট বেঁধে বেদনা জাগিয়ে দিয়ে গেলি। মনে পড়ল আমার সব ছিল-স্বামী-পুত্র, বিষয়-বৈভব সব। কিন্তু ভগবান সব কেড়ে নিয়েছিলেন। দেখছি মায়ার বন্ধন কাটে না, কাটতে গেলে প্রহ্লাদের মত হয়ে ওঠে। তাই শেষ সময়ে তুই যদি একবার আসিস, তবে তোকে দেখতে দেখতে চোখ বুজি।
ঠাকুরমার নিজের হাতে লেখা চিঠিখানা আমি নিজের কাছে রেখে দিলাম; সঙ্গে কৃষ্ণভামিনী কুঞ্জের কর্মচারী যে পত্র লিখেছেন, সেখানা তোমার কাছে পাঠালাম। পড়ে দেখো। এবং আমরা কালই রওনা হচ্ছি বৃন্দাবন। বন্দনার বরকে অথবা আমার ভাইকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হব। ঠাকুরমাও যাচ্ছেন সে নিশ্চয় বুঝতে পারছ। ইতি—
অৰ্চনা
* * *
হরিদ্বার থেকে বৃন্দাবন খুব বেশী পথ নয়, সেই দিন রাত্রে রওনা হয়ে ভায়া দিল্লী—পরের দিন দুপুরবেলা পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। যাওয়ার পথে একটা তাড়া ছিল সুলতা। তাড়া ওই ঠাকুরমার চিঠির কথাগুলি। “হঠাৎ তুই বার-দুই এসে ঠাকুমা বলে ডেকে নতুন করে রায়বাড়ীর ছেঁড়া বাঁধনে গিঁট বেঁধে বেদনা জাগিয়ে দিয়ে গেলি।” ওঁর পৈতৃকধন ছিল-তার মূল্য লাখ টাকার বেশী; সে-ও জ্যেঠামশায় এবং বাবা ওঁর হাত থেকে বের করে নিয়েছিলেন। এই সৰ্ববঞ্চিতা মহিলাটির বুকভরা ভালবাসা সারাজীবনে মানুষকে দেওয়া হয় নি—দিয়েছেন পাথরের দেবতাকে; এবং নিত্যই দেখেছেন এবেলায় দেওয়া তাঁর সে ভালবাসা পাথরের ঠাকুরের পায়ে দেওয়া ফুলের মতো ও-বেলায় বাসী হয়ে শুকিয়ে গেছে এবং তাকে ঘর থেকে বের করে বাইরে বিলিয়ে দিয়েছে কিংবা ফেলে দিয়েছে। সারাটা পথ সেকালের সেই অতিসুন্দর সুপুরুষ বিদগ্ধ দেবেশ্বর রায়কে মনে মনে শুধু তিরস্কারই করেছি।
মথুরায় নামতেই একটি স্বাস্থ্যবান দীর্ঘাকৃতি জোয়ান ছেলে এগিয়ে এল ছেলেটির রঙটা কালো, বেশ কালো নইলে হয়তো অনায়াসে মনে করতাম অর্চনার ভাই, হঠাৎ বড় হয়ে গেছে, চিনতে পারছি না। তার কারণ, ভদ্রলোকের দেহের গঠন যেমন শক্ত বলশালী, তেমনি লম্বা-চওড়া। আমাকে চিনতে তার খুব দেরী লাগে নি, আমার পরনে বাঙালী পোশাক ছিল, আমার ছবিও সে দেখেছে। এসে আমাকে প্রণাম করলে বললে, আমার নাম ললিত আচার্য। একটু বিস্মিত হলাম। নামটা ঠিক স্মরণ করতে পারলাম না। বিলেতে যখন আমি মদ্যপান করে ভেসে যেতে চাচ্ছি, তখনই অর্চনার চিঠিতে বন্দনার বিয়ের খবর পেয়েছিলাম। নামটা মনে রাখবার মত মানসিক সুস্থতা ছিল না, তবে পাত্রটির অসাধারণ পরিচয় আমার মনে ছিল। ছেলেটির বাপ ইস্কুলমাস্টারী করত, ম্যাট্রিকুলেশন পাস, সামান্য অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার, ছেলেটি বি-এ পাস করেছে অনার্স নিয়ে এবং সরকারী চাকরি পেয়েছে; এখন সে সার্কেল অফিসার। কীর্তিহাটের জমিদার কল্যাণেশ্বর রায় ধনেশ্বর রায়ের বিরুদ্ধে গোয়ানদের একটা দরখাস্তের তদন্তে এসেছিল। তারপর যাওয়া-আসা সূত্রে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। রায়বাড়ীতে তখন পাঁচ-সাতটি মেয়ে, তার মধ্যে বিবাহযোগ্যার থেকেও বেশী অরক্ষণীয়া দু-তিনটি। ছেলেটি অবিবাহিত। বন্দনাকে দেখে তার ভাল লেগেছিল। সে নিজেই লোক পাঠিয়ে সম্বন্ধ করে বন্দনাকে বিবাহ করেছে। পণ নেয় নি, যৌতুক চায় নি। অর্চনা নিজেই কিছু যৌতুক আর গহনা দিয়েছে। অর্চনা লিখেছিল—সুরোদা, রায়বাড়ীর মেয়েদের সম্পর্কে একটা অপবাদ আছে যে রায়বাড়ীর মেয়ের কপালে কখনও সুখ হয় না। যে সংসারে যায়, সে সংসার ভেঙে যায়; না গেলে মেয়ের কপাল ভাঙে। একা তো আমার নয়। অন্নপূর্ণা-মাও স্বামী নিয়ে ঘর করতে পান নি। তারপর জ্যাঠামশায়ের মেয়েদের দশা তো জান। তবু মনে হচ্ছে বন্দনার অদৃষ্ট ভাল হবে। বড়লোকের ঘর নয়; দালানবাড়ী নেই; কোনখানে পাপতাপ মাটিতে পুঁতে পাথর চাপা দেওয়া নেই। ছেলেটির নাম ললিত, ললিতের যেমন স্বাস্থ্য তেমনি চরিত্র, তেমনি বিনয় আর লেখাপড়ায় ভারী উজ্জ্বল; সরকারী চাকরি পেয়েছে; বন্দনা সুখী হয়ে চাকরির জায়গায় জায়গায় ঘুরবে। তবে জ্যাঠামশায় খুঁতখুঁত করেছিলেন—ছোটঘর, ছোটঘর, ঠিক হবে না, ঠিক হবে না বিয়ে দেওয়া, কিন্তু মা-জ্যাঠাইমা কেউ তাঁর কথা শুনলেন না। ছোটঘর কিসের? বিয়ে হয়ে গেল।
এ বিবরণটুকু মনে ছিল। তার সঙ্গে আর মনে ছিল বরের উপাধি হল আচার্য। ভদ্রলোক পাদপূরণ করে দিলেন, বললেন—আমি বন্দনাকে বিয়ে করেছি।
মনে পড়ে গেল, অর্চনার চিঠি, সে লিখেছিল বন্দনার বর বা ছোটভাইকে সঙ্গে করে কালই রওনা হব আমরা। আমি তাকে আর একবার ভাল করে দেখে সত্যি-সত্যিই বেশী করে খুশী হয়ে বললাম—কাছেই যমুনার ওপারে বৃন্দাবন, তোমাকে দেখে তো ভাই ইচ্ছে করছে না, তোমাকে ললিত বলে ডাকতে। ইচ্ছে করছে তোমাকে—
ছেলেটি হেসে বলল-মেজদি আমাকে কেলেসোনা বলে নতুন নামকরণ করেছেন বৃন্দাবনে পা দিয়েই।
আমি বললাম—না, কেলেসোনা বলে তোমায় ডাকব না ভাই। ওটা মেজদি বলেছেন—মেজদিকে সাজে। আমি তোমাকে শ্যামসুন্দর বলে ডাকব। ললিতের চেয়ে খারাপ লাগবে না।
ললিত হেসে উঠে বললে—তাই ডাকবেন।
* * *