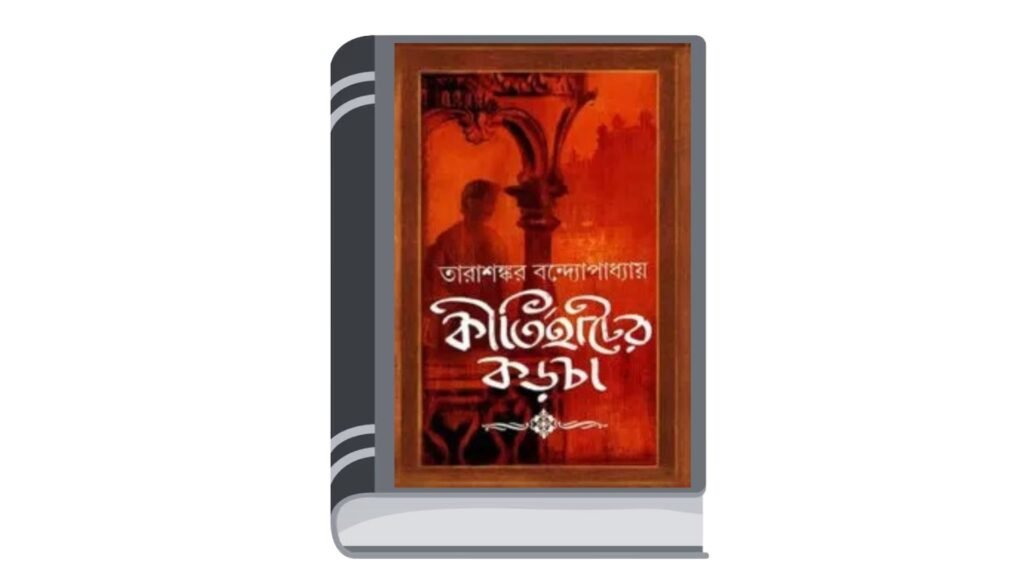কীর্তিহাটের কড়চা – ৪র্থ খণ্ড – ১৯
১৯
বৃন্দাবনের গাড়ীতে উঠে ললিত বললে—আপনাকে দেখবার আমার আগ্রহ ছিল দাদা। আমি চোখ বুজে সিগারেট টানতে টানতে ভাবছিলাম—একেই বলে ভাগ্য। আমি কত খুঁজে, কত অর্থব্যয় করে অর্চনাকে অন্নপূর্ণা-মায়ের নাতির ছেলে রথীনের মত ছেলের হাতে তুলে দিয়েছিলাম কিন্তু তাকে সুখী করতে পারি নি। আর বন্দনার ভাগ্য দেখ, কোথা থেকে এমন একটি গুণবান, সবল স্বাস্থ্যবান, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ছেলে পায়ে হেঁটে রায়বাড়ীতে এসে বন্দনাকে নিজে উপযাচক হয়ে বিয়ে করে নিয়ে গেল।
ললিত সারাটা পথ মথুরা থেকে বৃন্দাবন আমায় কি করে যত্ন করবে তা খুঁজে পাচ্ছিল না। আমি হেসে বলেছিলাম—ভাই ললিত, তুমি এত ব্যস্ত হলে তো আমাকে ব্যস্ত-ত্রস্ত এবং তার উপরে কিছু থাকলে তাই হতে হয়। তুমি আমার ভগ্নীপতি, আমি তোমার সম্পর্কে বড় হলেও শ্যালক। যাকে সোজা বাংলায় বলে তালব্য-শ-য়ে আকার ল-য়ে আকার। এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন তুমি?
ললিতের মধ্যে একটা সত্যকারের বিনয় ছিল। সে বললে—দেখুন দাদা, রায়বংশে বিয়ে করে আমি খুশী হয়েছি নিশ্চয় কিন্তু কল্যাণবাবু-টাবুকে আমার ভাল লাগে না; ওরা আমার এমন তোষামোদ করেন সার্কেল অফিসার বলে যে, লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়। এক অতুলকাকা আছেন যাঁকে শ্রদ্ধা-ভক্তি হয়। আমি সরকারী কর্মচারী, তিনি জেলখাটা স্বদেশী-করা মানুষ, তবু শ্রদ্ধা করি। গোপনে করি। প্রকাশ্যে শ্রদ্ধা খাতির করবার তো উপায় নেই। তার উপর মেদিনীপুর। আর শ্রদ্ধা করি আপনাকে। আগে শুনে শ্রদ্ধা করতাম। আজ দেখে শ্রদ্ধা হচ্ছে।
কি উত্তর দেব? উত্তর কিছু দিলাম না, চুপ করে চোখ বুজে সিগারেট টানছিলাম।
ললিত একটু চুপ করে থেকে বললে—জানেন, কীর্তিহাটের রায়বংশের এত গল্প আমি ছেলেবেলা থেকে শুনেছি। সে একটা ড্রিমল্যান্ড বা ফেয়ারী কিংডমের ব্যাপারের মত। আমার ঠাকুমা বলতেন। তিনি গল্পগুলো শুনেছিলেন তাঁর শাশুড়ীর কাছে। শ্বশুরের কাছে। আমাদের তখন বাড়ী ছিল আপনাদেরই জমিদারীর মধ্যে। তখন আপনাদের বংশের মালিক ছিলেন রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় দি গ্রেট। আমার ঠাকুমা বলতেন—তাঁর ভয়ে বাঘে-বলদে এক ঘাটে জল খেতো। বলতেন, আমার শ্বশুর কি একটা অপরাধ করে ফেলেছিলেন; তারপর এমন ভয় হল যে, আর রায়বাহাদুরের এলাকায় থাকতে সাহস হল না। তখন আমার ঠাকুরদা তিন মাসের কচি ছেলে। ঠাকুরদার বাবা রায়বাহাদুরের ভয়ে যা জমিজমা ছিল, সব বেচেবুচে স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন গ্রাম থেকে। ঠাকুরদার মা ঠাকুরদাকে বুকে চেপে ধরে কাঁদতে কাঁদতে এসেছিলেন সারা রাস্তাটা। মেদিনীপুর থেকে পালিয়ে এসেছিলেন হাওড়াতে। সালকের দিকে গঙ্গার ধারে ছোট ছিটেবেড়ার ঘর বেঁধে বাস শুরু করেছিলেন।
আমার চোখ দুটো আপনি খুলে গিয়েছিল।
আমি নিষ্পলক দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। আচার্য? কোন্ আচার্য? রায়বাহাদুর রত্নেশ্বরের আমলে তাঁর শাসনের ভয়ে কোন্ আচার্য তাঁর স্ত্রীর হাত ধরে গ্রাম পরিত্যাগ করে পালিয়ে এসেছিল?
ললিত বলছিল—আপনাদের বংশের রূপের খ্যাতি শুনেছিলাম। শুনতাম আর সাধ হত আপনাদের দেখতে। আমার ঠাকুরদার বাবাকে রায়বাড়ীর কাছারীতে ডাকা হয়েছিল। ভয়ে তাঁকে একলা যেতে দেন নি আমার ঠাকুরদার মা। কচি ছেলে কোলে করে তিনি স্বামীর সঙ্গে গিয়েছিলেন। কীর্তিহাটের কালীমন্দিরের সামনে নাটমন্দিরে দাঁড়িয়ে তিনি স্বামীকে আগলে ছিলেন। আমার ঠাকুরদা খুব কালো ছিলেন, একেবারে নিকষ কালো। ঠাকুরদার মা বলতেন—ব্যবসাবাণিজ্য করে ছেলে আমার খুব বড়লোক হবে, তখন রায়বাড়ীতে বিয়ে দিয়ে সুন্দর বউ আনব। কালো রঙের দুঃখ ঘুচবে।
সে বকেই যাচ্ছিল, বকেই যাচ্ছিল। লেখাপড়া-জানা ভাল ছেলে, বুদ্ধিমান ছেলে, সরকারী চাকরি করে; তবু আনন্দবিহ্বল ছোটছেলের মত বকেই চলেছে, বকেই চলেছে। সে আনন্দে তার কোন কলুষ ছিল না, কুটিলতা ছিল না। না—একবিন্দু এতটুকু কিছু ছিল না।
আমার মনে পড়ছিল, অন্নপূর্ণা-মায়ের কাছে পাওয়া দেবেশ্বর রায়ের লেখা একখানা চিঠির কথা। যে-চিঠিতে তিনি রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের নিষ্ঠুর চরিত্রের কথা লিখতে গিয়ে দুটি ঘটনার কথা লিখেছিলেন। একটি ঘটনা, কীর্তিহাটের নিকটবর্তী গ্রামের এক পঙ্গু আচার্য ব্রাহ্মণ এবং তাঁর যুবতী স্ত্রী শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদেছিল। ক্ষমার অযোগ্য সামাজিক অপরাধের জন্য রায়বাহাদুর হুকুম করেছিলেন, গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে। ওই মেয়েটির কোলের ছেলেটি কষ্টিপাথরের মত কালো ছিল এবং সবল-সুস্থ ছিল তার স্বাস্থ্য।
এই ললিত আচার্য—আজ রায় রত্নেশ্বর রায়বাহাদুরের প্রপৌত্রী বন্দনাকে বিবাহ করলে, সে কে?
আর একটি ঘটনার কথা লিখেছিলেন। সেটি দেবেশ্বর রায়ের ভিক্ষে-মা, জাতিতে কায়স্থ, বিধবা কৃষ্ণভামিনী দাসীর কথা।
তাঁর অপরাধের জন্য রায়বাহাদুর তাঁকে দেশ থেকে নির্বাসিতা করেছিলেন। আজ বৃন্দাবনে কৃষ্ণভামিনীর সেবাকুঞ্জে আশ্রয় নিয়ে শেষ শয্যা পেতেছেন রায়বাহাদুরের পরমাদরের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ দেবেশ্বর রায়ের পত্নী আমার ঠাকুমা।
ভাবছিলাম, রায়বাড়ীটা কি আজ এই মুহূর্তে ভূমিকম্প হয়ে চুরমার হয়ে মাটির উপর একটা ইট-চুন-সুরকি-ভাঙা কাঠকাঠরায় ধ্বংসরূপে পরিণত হয়ে গেল?
সেদিন মনে মনে কামনা করেছিলাম—এই মুহূর্তে একটা ভূমিকম্প হোক এবং সেই ভূমিকম্পে কীর্তিহাটের রায়বাড়ী ভেঙে চৌচির হয়ে আছড়ে পড়ে চুরমার হয়ে যাক। তার মধ্যে রায়বংশধরেরা চাপা পড়ে শেষ হয়ে যাক। ওদের কাজ শেষ হয়েছে। কৃষ্ণভামিনীর দেহ এবং নাচগান বিক্রী করা অর্থে গড়া কৃষ্ণভামিনী সেবাকুঞ্জে দেবেশ্বর রায়ের স্ত্রী শেষ শয্যা পেতেছে; এবং যে ব্রাত্যজনসংসর্গজাত সন্তানের জননী এবং পুরুষত্বহীন জনককে নির্বাসিত করেছিলেন রত্নেশ্বর রায়, তারই পৌত্রের সঙ্গে রত্নেশ্বর রায়ের প্রপৌত্রীর বিবাহ হয়, সম্প্রদানের সময় এই ললিতের পা ধরে অর্চনা করে বলা হল, হে বিশিষ্ট বর, তোমাকে কন্যাদান করছি, তুমি গ্রহণ কর। ব্যাস্, আর বাকী কি রইল। সব শেষ হয়ে গেল —এবার ছেদ পড়ে যাক। এবং বেশ একটা টেম্পোর মাথায় পড়ুক, ভূমিকম্প হোক—। কিন্তু তা হল না। কারণ ইচ্ছে করলেই কিছু হয় না। তবে ধাক্কাটা লেগেছিল। প্রথমটা যথেষ্ট লেগেছিল। সামলাতে বেগ পেয়েছিলাম।
অর্চনা বার বার জিজ্ঞাসা করেছিল—কি হয়েছে সুরোদা? শরীর খুব খারাপ? চিঠিপত্রেও যা লেখ তাও যেন কেমন কেমন, এতকাল পর এলে কিন্তু—। কথা সে খুঁজে পেলে না একটুক্ষণ চুপ ক’রে থেকে বললে—তুমি যেন কেমন হয়ে গেছ।
কথাটার জবাব দিতে পারি নি, হাসি দিয়ে অপ্রিয় প্রসঙ্গ চাপা বা ঢাকা দেওয়া যায়, মানুষে দিয়েও থাকে, সেদিন আমি তা দিতে পারি নি। সত্য কথাটা বলবার মতোও বুকে জোর ছিল না, সুতরাং চুপ ক’রেই ছিলাম। অর্চনা তখনও জানত না আচার্যের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে পিতামহের বাপের সঙ্গে রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের আসল সংঘর্ষের কথা।
বলতে বলতে থামল সুরেশ্বর। তখন দিনের আলো বেশ ফুটে উঠেছে দিনের আলো কেন রোদ্দুরও ফুটেছে। নিচে ফ্রী স্কুল স্ট্রীট ধরে যানবাহন লোকজন চলাচলের বিচিত্র মেলানো-মেশানো সাড়া উঠেছে; ট্যাক্সির হর্ন, প্রাইভেটের ইলেকট্রিক হর্ন; ফ্রী স্কুল স্ট্রীট অঞ্চল ফিটনের আড়ত—ফিটনের ঘণ্টার শব্দ, মধ্যে মাঝে গরু মোষের গাড়ী, রিকশার ঘণ্টা, ঠেলার হুঁশিয়ারি মানুষে মানুষে সংঘর্ষের কলহের হাঁক একসঙ্গে মিশে চলমানতার গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠেছে। সুরেশ্বর থামল। বাইরের জানালার দিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে বললে-সামলাতে প্রায় একটা বেলা লেগেছিল। ঠাকুমার শেষ প্রায়শ্চিত্ত দেখে এবং শুনে মনের ক্ষোভটা গেল।
তুমি হয়তো জানো—জানো বলেই ধরে নিচ্ছি, জানো না বলে তোমাকে খাটো করব কেন? আমাদের দেশ হিন্দুসমাজে নানান সংস্কারের মধ্যে মৃত্যুর পূর্বে প্রায়শ্চিত্তের একটা বিধি আছে। মানুষ দীর্ঘস্থায়ী রোগে ভুগছে, মরণ হচ্ছে না, এমন অবস্থায় মানুষ প্রায়শ্চিত্ত করে, নারায়ণকে ঘটে হোক শিলারূপে হোক সামনে রেখে জীবনের পাপ স্মরণ করে বলে—“ক্ষময়া ক্রিয়তে পাপং”–যে পাপই করে থাকি সে গুরুই হোক আর লঘুই হোক সে সবই তুমি মার্জনা কর। ক্রীশ্চানদের কনফেশনের সঙ্গে এর একটা মিল আছে।
ঠাকুমা—দেবেশ্বর রায়ের স্ত্রী বড় দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন—অসুখ দেখানোর মত কিছু ছিল না, ক্রমশ ক্রমশ মৃত্যুর দিকে চলছিলেন কিন্তু গতিটা নেহাতই পিঁপড়ের গতির মতো। তাই তিনি এই প্রায়শ্চিত্ত করলেন সেদিন।
আয়োজন হয়েই ছিল কিন্তু সকাল থেকে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বলে অনুষ্ঠান হয়নি; তাঁর চেতনা হলে সেই অনুষ্ঠান আরম্ভ হল। পুরোহিত এসেছিল কিন্তু ফিরে গিয়েছিল ঠাকুমাকে ঘুমন্ত দেখে। এবং ঠিক হয়েছিল যদি এরই মধ্যে ‘কোমা’ এসে যায় তবে মেজঠাকুমা বাঁ হাতে বড় ঠাকুমাকে ধরে তাঁর হয়ে মন্ত্র পড়বেন, ভোজ্য দান ইত্যাদি যা উৎসর্গ করবার তা উৎসর্গ করবেন।
আমি বসে ভাবছিলাম বৃন্দাবনে এই কৃষ্ণভামিনীর কুঞ্জে বসে মদ্যপান আমি করতে পারি কিনা? করলে বাধা কে দেবে? যিনি দিতে পারেন বা পারতেন আমার ঠাকুমা তাঁর একরকম জ্ঞান নেই। হতচেতনের মতো ঘুমুচ্ছেন। কিন্তু আমি যেন অধিকার মানে রাইট খুঁজে পাচ্ছিলাম না।
এসে ডাকলে অর্চনা। এসো সুরোদা, ঠাকুমার চেতন হয়েছে, একটু যেন সুস্থ হচ্ছে, বলছেন—প্রায়শ্চিত্ত এখুনি করব। পুরোহিত চলে গেছে, মুশকিল হয়েছিল কিন্তু বন্দনার বর ললিত বললে—আমি করিয়ে দিচ্ছি দিদি। আমি এককালে বাবার কাছে এসব কাজ শিখেছিলাম বাবা ইস্কুলে পণ্ডিতি করতেন আর পুরুতের কাজও করতেন। আমার স্যুটকেসে বইও আছে।
গেলাম। মনের মধ্যে যে একটা অস্বস্তি একটা বেদনা ঘুরপাক খাচ্ছিল এই মুহূর্তে সেটা চরমে উঠল। অথচ আমি আধা-ইংরেজ যোগেশ্বর রায়ের ছেলে, নিজে একসময় বাবা-মাকে এবং আমাকে যে দুঃখ দিয়েছিলেন তার জন্য পৈতের পর কিছু গোঁড়া ব্রাহ্মণ হতে চেষ্টা করেছিলাম—কিন্তু তা রাখতে পারি নি, কিছুদিন যেতে না যেতেই একেবারে আল্ট্রামডার্ন হয়ে উঠেছিলাম। জাতধর্ম ঈশ্বর পরলোক সব লোককে অবিশ্বাস করে বিলুপ্ত করে দিয়েছি, মানি না। দেবতা দেবলোক যেটুকু মানি সে মানি দেবোত্তর সম্পত্তির জন্য এবং এখনও এদেশে ব্রাহ্মণবংশের রক্তের একটা অ্যারিস্টোক্রেসি আছে তার জন্য, নিজে ইংরেজের দেশে গিয়েছিলাম ইংরেজ-ললনার দেহসরোবরে ডুবে মরতে। কিন্তু মরতে পারি নি। শম্পা রায় নামধারিণী লরার দেহসরসীতে তাকিয়ে ভয় পেয়েছিলাম—মনে হয়েছিল ভয়ঙ্কর অপমৃত্যু উঁকি মারছে।
নরকের ভয় নয়, নরক একালে কেউ মানে না, আমিও মানি না, তবু ওটাকে বড় ভালগার অশ্লীল মনে হয়েছিল তাই পালিয়ে এসেছিলাম। ইউরোপে যুদ্ধ লেগেছে, নাহলে হয়তো ফ্রান্স বা ইটালিতে যেতাম মরণ-সরোবরের সন্ধানে। শেষে পালিয়ে এলাম। সে কি এই দেখতে এলাম?
দেবেশ্বর রায়ের অবহেলিত গৃহিণী মরছেন কৃষ্ণভামিনীর সেবা-কুঞ্জে আর তাঁর মৃত্যুকালে প্রায়শ্চিত্ত করাচ্ছে ললিত আচার্যি! ললিত আচার্যি—অন্নপূর্ণা-পিসীকে লেখা দেবেশ্বর রায়ের চিঠিখানা আমার মনে পড়ছে।
নিয়তি বা ভগবানের বিচার এ আমি মানি না। এ তা নয় তাও জানি। এমনটা নেহাতই ঘটনাচক্র। এর পিছনে কোন ত্রিকালের বিধাতার প্ল্যানিং নেই। তবে একটা জিনিস আছে সেটা হ’ল এই নিজে না থামলে কেউ রুখতে পারে না। এবং সংসারে পাপকে পিছনে ফেলে এগিয়ে এলেই তুমি মুক্ত।
অর্চনা বুঝতে পারছিল একটা খোঁচায় আমি অস্বস্তি ভোগ করছি; সেটা কি তা ঠিক ধরতে পারে নি। সে বলেছিল-তোমার কি হয়েছে আমাকে বলবে না?
বললাম—বলব পরে। এখন না। চল এখন। বলে পা বাড়ালাম। এসে দাঁড়ালাম প্রায়শ্চিত্তের জায়গায়। কি বলব তোমাকে সুলতা, এসে দাঁড়িয়ে একবার তাকিয়ে দেখে মনটা যেন জুড়িয়ে গেল। সত্যি-সত্যিই সে যেন একটি মুক্তিযজ্ঞের আসর পাতা হয়েছে।
ঠাকুমাকে গরদের কাপড় পরিয়েছে—তিনি বসেছেন মেজদিদির উপর দেহের ভার রেখে; ঠাকুমা মানুষটি বরাবরই ছোটখাটো, বয়স হয়ে আরও ছোট হয়ে গেছেন; আর আমার মেজদিদি মাথায় বেশ লম্বা এবং বন্ধ্যা নারী, তাঁর দেহখানির বাঁধুনি বেশ শক্ত, তিনি তাঁকে পিঠের দিকে জড়িয়ে ধরে বসেছেন।
সামনে আসনের উপর বসেছে জামাই ললিত আচার্য। ধবধবে কাচা কাঁচি ধুতি পরনে গায়ে সিল্কের চাদর, গাঢ়-শ্যাম গায়ের রঙ, তার উপর সাবানে পরিষ্কার করে কাচা খরখরে মোটা পৈতে, চোখে চশমা-ছ-ফিট লম্বা সবল স্বাস্থ্যবান যুবা, সোজা মেরুদণ্ড, বসে নিপুণ পুরোহিতের মত সামনে রাখা ভোজ্য এবং দানগুলির পাত্র পরের পর সাজিয়ে রাখছে। এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই ভরাট গলায় সে মন্ত্র উচ্চারণ করাতে শুরু করলে, বলুন—কোশাতে—হ্যাঁ।
তখন রায়বাড়ীর বড়বউ কোশাতে হরিতকী ধরে হাতের উপর হাত রেখেছেন। ঠাকুমাকে দেখলাম কপালে গঙ্গামৃত্তিকার তিলক এঁকেছেন—একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন সামনের দিকে। বলুন—ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু! ওঁ তদ্বিষ্ণু পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবীবচক্ষুরাততং—ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু।
গম গম করে উঠল স্থানটি, যেন অনুষ্ঠানটি সজীব প্রাণময় হয়ে উঠল; আশ্চর্য একটা সঙ্গীত যেন সৃষ্টি করলে ললিত তার ভরাট কণ্ঠস্বরের মহিমায় আর তার জিহ্বার অতি পরিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণে।
আমি আজও মনে করতে পারছি, চোখের উপর স্পষ্ট ভাসছে সমস্ত; কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি অনুষ্ঠানটির প্রভাবে অভিভূত হয়ে গেলাম। পরলোক, স্বর্গ নরক বাদ দাও, আমার মন যেন পবিত্র হয়ে গেল, একটি উদাসীনতা চিত্তকে স্পর্শ করলে, আমার মনের সব উত্তাপ সব ক্ষোভ যেন জুড়িয়ে জল হয়ে গেল।
সেদিন রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইন—“অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত, তুমি দ্বিজোত্তম তুমি সত্যকুলজাত” অংশটুকুও মনে পড়ে নি। শুধু মনে মনে মেনে নিয়েছিলাম এ অব্রাহ্মণ হলে ব্রাহ্মণ আর দেশে সমাজে নেই। মুক্তি যদি এই অনুষ্ঠানে মেলে তবে এই ছেলেটির চেয়ে শুদ্ধ এবং সিদ্ধ পুরোহিত আর দেশে নেই।
ঠিক এই সময়ে আর একটা ঘটনা ঘটেছিল সুলতা। ঠাকুমা মন্ত্র পড়তে পড়তে তাঁর দৃষ্টি ফিরিয়ে আমাকে দেখে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলেন। চোখের দৃষ্টি বিস্ময়-বিস্ফারিত হয়ে গেল, কপালের কুঞ্চনরেখায় মনের অনুচ্চারিত প্রশ্ন ফুটে উঠল শিলালিপির মত; তারপর কাঁপতে শুরু করলেন।
ললিত তখন ব’লে যাচ্ছিল—ওঁ অদ্য মার্গশীর্ষে মাসি শুক্লে পক্ষে ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ শাণ্ডিল্য গোত্ৰ—
ললিত একটি একটি ক’রে সংস্কৃত শব্দগুলি উচ্চারণ করছিল, ঠাকুমা একটি একটি ক’রে উচ্চারণ ক’রে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ বলার পর তিনি চোখ তুলে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। চোখ যেন বিস্ময়-বিস্ফারিত, পুরু চশমার ওপাশে চোখ দুটিকে খুব বড় এবং খুব বেশী বিস্ফারিত মনে হচ্ছিল, দন্তহীন মুখ খানিকটা হাঁ হয়ে গেছে। তিনি একটু একটু কাঁপছেন। মনে হচ্ছে একটা কিছু হয়েছে। সে একটা কিছুর অর্থ, ওই স্থানকালপাত্র বিচার করলে চরম মুহূর্তের মুখোমুখি দাঁড়ালাম বুঝি বলে আশঙ্কা হয়। সবাই আমরা সেই আশঙ্কাই করেছিলাম। কি হল?
ললিত একটু ঝুঁকে বললে —বলুন —তিথৌ —।
অর্চনা সামনে হেঁট হয়ে ডাকলে-ঠাকুমা! ঠাকুমা!
পিছন থেকে মেজদিদি বললেন-কর্তাদিদি! দিদি—গায়ে একটু নাড়া দিলেন। দিদি! হঠাৎ যেন সচেতন হলেন ঠাকুমা, তাঁর বাঁ হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন—ছাড়, ছাড়। আঃ, ঘোমটা দিতে দে। দেখছিস না বড়বাবু দাঁড়িয়ে। ছাড়।
বড়বাবু মানে দেবেশ্বর রায়। আমরা চমকে উঠেছিলাম। কোথায় কি দেখছেন—কাকে দেখছেন?
মেজদিদি তাঁর কানের কাছে মুখ এনে বললেন —না—না—উনি বড়বাবু নন। সুরেশ্বর, ও সুরেশ্বর—নাতি আপনার নাতি। বড়দি―!
আমার মনে পড়ে গেল আমি দেখতে আমার পিতামহ দেবেশ্বর রায়ের মত। আমি নিজে এগিয়ে গিয়ে তাঁর কাছে এসে ডাকলাম—ঠাকুমা, আমি সুরেশ্বর!
—সুরেশ্বর? কে সুরেশ্বর!
ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। আমি বললাম—মন্ত্র বলুন- প্রায়শ্চিত্ত শেষ করুন।
এবার সম্বিৎ ফিরে পেলেন, বললেন-ও হ্যাঁ, কি বলব?
ললিত বললে-আবার বিষ্ণু স্মরণ করে নিন, আগে বলুন- শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু। নমঃ তদবিষ্ণু পরমং পদং—
আর ভুল হল না ঠাকুমায়ের-তিনি প্রায়শ্চিত্ত করে গেলেন একটানা। প্রায়শ্চিত্ত করতে করতে চোখ থেকে জলের দুটি ধারা নেমে এল।
তিন দিন পর মারা গেলেন ঠাকুমা—দেবেশ্বর রায়ের গৃহিণী—উমা দেবী। মারা যাওয়া তাকে বলে না, যেন চোখ বুজে ঘুমোলেন। কেউ ভাবতে পারে নি যে আর তিনি চোখ মেলবেন না। কারণ প্রায়শ্চিত্ত শেষ করে রাত্রি থেকে এমন সহজ আর সুস্থ তিনি হয়ে উঠেছিলেন যে আমরা ভেবেছিলাম তিনি হয়তো নতুন ক’রে বাঁচলেন। নতুন ক’রে বাঁচাই বটে। কারণ পুরনো কথাগুলো যা তিনি বিস্মৃত হয়েছিলেন—যা কেউ জানত না আমাদের মধ্যে—সেই সব কথা বলতে লাগলেন। হাসলেন। আমাকে ললিতকে সমাদর করলেন; অর্চনাকে দেখে দিদিশাশুড়ী ভবানী দেবীকে স্মরণ করে বললেন—কিন্তু ভাই, এমন দুঃখভোগ করবার জন্য তো তাঁর ফেরার কথা নয়। দুঃখ পেয়ে গিয়েছিলেন—সুখ করবার জন্য ফিরে আসবার কথা। তা হ’লে? তা হ’লে কেন এমন হল তোর?
আর সময় পেলেই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। বলতেন—অবিকল আমার বড়বাবু। তফাৎ বড়বাবুর মোম দিয়ে পাকানো গোঁফ ছিল। মাথায় আলবার্ট তুলে টেরি কাটতেন, আর ভয়ানক বাবু ছিলেন। চব্বিশ ঘণ্টা আতরের গন্ধে ম-ম করত। মনে হচ্ছে তিনিই তুই হয়ে ফিরে এসেছেন নিজের দেনা শোধ করতে। দেনা যে অনেক। দেখ না ভাই, নইলে শেষকালটায় আমার মৃত্যুশয্যায় তুই বসে থাকলি কেন? আমার বড় ছেলে—।
জ্যাঠামশায় যজ্ঞেশ্বর রায়, তাঁর পৈতৃক এক লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ নিয়ে নিয়েছিলেন, তিনি সকলের অজ্ঞাতসারে বাড়ী ছেড়ে বৃন্দাবন এসে ভিক্ষে-শাশুড়ী কৃষ্ণভামিনী সেবাশ্রমে আশ্রয় নিয়েছিলেন ব’লে। তিনি আসেন নি। আসতে সম্ভবত লজ্জা পেয়েছিলেন।
তাই কথাটা বললেন ঠাকুমা।
নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন —আমার মুখের আগুনও তোকেই দিতে হবে। দেনা শোধ রে, দেনা শোধ। তা ভাই এক কাজ করিস। সারাজীবন তো মানুষকে না পেয়ে ভগবান আর দেবতাকে নিয়ে থাকলাম, ভাগবত পুরাণ অনেক পড়েছি। তোদের বংশের দেনাগুলো শোধ করিস। দেনা অনেক অনেক—অনেক। হয় না শোধ। জানতেই পারবিনে। তবে যা জানতে পারবি তা শোধ করিস। তোর কাছেই তো শুনেছি দরপত্তনীতে পত্তনীতে রায়বাড়ীর সব জমিদারী এসে জমা হয়েছে। তুইই তো আসল মালিক। শোধ করিস—
অর্চনা পাশে বসেছিল, সে হঠাৎ বলে উঠল—সুরোদা যে জমিদারী সম্পত্তি সব বেচে দেবে ঠিক করেছে।
—বেচে দেবে? চমকে উঠলেন ইলেকট্রিক শক খাওয়া মানুষের মত। বেচে দেবে? কি বেচে দেবে?
—জমিদারী।
—জমিদারী বেচে দেবে?
আমার চোখের দিকে চোখ রেখে তিনি তাঁর প্রশ্নের উত্তর চেয়েছিলেন আমার কাছে। উত্তর দিতে দেরী হয়েছিল আমার; তিনি খানিকটা অধীর হয়েই বলেছিলেন-বেচে দিবি? হাঁ রে! রায়বংশ—আর কথা খুঁজে পান নি।
অৰ্চনাই বলেছিল—যে সব পাপের কথা বলছ ঠাকুমা তা সুরোদা জানে। পুরনো কাগজ ঘেঁটে ঘেঁটে বের করেছে। ওই জন্যেই বেচে দেবে। জমিদারী রাখতে হলে নানা অন্যায় করতে হয় বলে প্রজাদের দান করে দেবে।
অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিলেন—দেখ, জমিদার রাজা, এরা হল ইন্দ্রদেবতার জ্ঞাতগোত্র রে। এদের এ না করে উপায় নেই। দেখ না ইন্দ্ররাজা স্বর্গের রাজা; রাজ্য করতে গিয়ে তাকে কত কি করতে হয়েছে। ভেবে দেখ, ব্রহ্মহত্যা করেছে, নারীহরণ করেছে। মুনিঋষিদের অপমান করেছে; রাজ্য করতে গেলেই ওসব করে। কিছু করে কিছু করতে হয়; করেছে; অভিশাপও খেয়েছে, কত লাঞ্ছনা হয়েছে, হাজারটা চোখ হয়েছে; প্রায়শ্চিত্ত করেছে; রাজ্য হারিয়ে আবার রাজ্য পেয়েছে। তা বলে তো বেচে দেয় নি রে! তুই বেচে দিবি?
ললিত ঠাকুমার কথা শুনে খুব তারিফ ক’রে বলেছিল—ঠাকুমা বড় চমৎকার কথা বলেছেন দাদা। ভারী চমৎকার! রাজা—সে ইন্দ্র থেকে দৈত্য দানব রাক্ষস মানুষ জন্তু-জানোয়ার যেই হোক তার অত্যাচারী না হয়ে উপায় নেই। কুটিল পথ ছাড়া তার পথ নেই। পৃথিবীতে পূজা সে পৃথক ভাবে পায় না। দশ দিকপালের মধ্যেই যা পাবার পায়। তার বেশী নয়। তবু ইন্দ্রত্বের চেয়ে কাম্য কিছু নেই। শতকরা নিরেনব্বুইজন তপস্যা করে ইন্দ্রত্বের জন্য। বড় জোর একজন চায় ভগবান কিংবা মুক্তি। তাই কেউ তপস্যা করলেই ইন্দ্র তাকে ধ্বংস করতে চায়।
ললিত সংস্কৃতের ভাল ছাত্র, সংস্কৃতে এম-এ পাস করেছিল। সে পুরাণ থেকে ইন্দ্রতত্ত্ব বোঝাতে শুরু করেছিল। সেসব কথা ভুলে গেছি, একটা কথা মনে আছে বলেছিল—এক রাম ছাড়া কোন রাজা প্রজার পরম ভক্তি পান নি। অন্যদের ভয় করেছে, ঘৃণা করেছে, সেলামী নজরানা দিয়েছে, পূজো করে দেয় নি। ওই এক রাম ছাড়া। এর জন্য রামকে সীতা বিসর্জন দিয়ে মূল্য দিতে হয়েছিল।
ঠাকুমা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—ভেবে দেখিস ভাই। এত বড় রায়বংশের সন্তান তুই—বড় রায়ের পৌত্র, রায়বাহাদুরের প্রপৌত্র, ওরে তোকে তোর বংশাবলীকে কেউ আর গ্রাহ্য করবে না; দেখলে মাথা নোয়াবে না। ওরে তোকে কীর্তিহাট ছেড়ে পালিয়ে আসতে হবে।
আমার মনে সেদিন যেন একটা কান্নার আবেগ বর্ষার মেঘের মত ফুলে ফুলে উঠছিল। বর্ষণ হয় নি, হ’তে দিই নি, বহু কষ্টে আত্মসম্বরণ ক’রে বসে ছিলাম। মনে হচ্ছিল কীর্তিহাটের রায়বাড়ীর জমিদারীর অতি বৃদ্ধা প্রাণপ্রতিমা বলছেন—বেচে দিয়ো না, আমাকে বেচে দিয়ো না।
* * *
চুপ করে গেল সুরেশ্বর। একটু পরে একটা সিগারেট ধরিয়ে বিষণ্ণ হেসে বললে—দেখ ছোটবেলায় পড়েছিলাম —’বীরবল কথা’—বীরবল ছিলেন দুঃসাহসী যোদ্ধা। এক রাজার রাজ্যে কাজ করতেন। মাইনে নিতেন খুব বেশী। বলেছিলেন—যা কেউ না পারবে তাই সে করবে। রাত্রে রোজ রাজপুরীতে সারারাত্রি জেগে পাহারা দিতেন। হঠাৎ একদিন শুনলেন রাজপুরী থেকে কেউ কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে আসছে। তিনি ভয় পেলেন না, এগিয়ে গেলেন। দেখলেন একজন সুন্দরী নারী কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে আসছেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন- তুমি কে মা? কেন কাঁদছ তুমি?
মেয়েটি বললে—আমি রাজলক্ষ্মী, এই রাজাকে আজ পরিত্যাগ ক’রে যেতে হচ্ছে ব’লে কাঁদছি। দীর্ঘকাল একে আশ্রয় ক’রে ছিলাম, রাজাকে বড় ভালবাসতাম স্নেহ করতাম—তাই বুকটা টনটন করছে।
বীরবল জিজ্ঞাসা করলেন—কি অপরাধে রাজাকে ত্যাগ করবে মা?
রাজলক্ষ্মী বললেন—রাজার আজ রাত্রি অবসানে পরমায়ুর শেষ হবে। রাজার যিনি পুত্র তাঁর ভাগ্যে রাজ্য নেই।
বীরবল জিজ্ঞাসা করেছিলেন—রাজাকে কি কোন উপায়ে বাঁচানো যায় না মা!
—যায়। যদি কেউ শ্মশানে যে মহাকালী আছেন তাঁর ওখানে গিয়ে নিজের মুণ্ড কেটে মায়ের পূজো দেয় তবে রাজা তাঁর পরমায়ু নিয়ে বাঁচতে পারেন।
বীরবল বললেন—মা, তা হলে তুমি ফিরে যাও মা। আমি এই রাজার ভৃত্য। তাঁকে মৃত্যুমুখ থেকে সাধ্য হলে জীবন দিয়ে রক্ষা করাই হল যোদ্ধা ভৃত্যের কর্তব্য। সে কর্তব্য আমি পালন করব মা। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে ফিরে যাও।
রাজলক্ষ্মী তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন, অন্তঃপুরের দিকে।
ঠিক সেই গল্পের বীরবলের মতই আমি সেদিন ঠাকুমার কাছে সেই আবেগের বশে বলেছিলাম—আমি কথা দিচ্ছি ঠাকুমা, আমি জমিদারী বেচব না। রাখব।
সে প্রতিশ্রুতি সেদিন যার হিসেব জ্ঞান আছে তার কাছে বড় সহজ ছিল না, এ কথা আমার থেকেও বোধ করি তুমি অনেক ভাল করে জান এবং তার ভিতরের কারণ বোঝো। জমিদারীতে জমিদার সেদিন নিতান্তই পুতুল মালিকের মত মালিক হয়েছে।
প্রজারা তখন জমিদারদের থেকে অনেক বেশী শক্তিমান হয়েছে। যে রাষ্ট্র জমিদারী সৃষ্টি করেছিল সেই রাষ্ট্রই সেদিন দুর্বল হয়ে গেছে দেশের মানুষের কাছে, সুতরাং জমিদারদের অবস্থা হয়েছে প্রায় গাছতলায় পড়ে থাকা হাত-পা-ভাঙা নাক-কাটা পাথরের মূর্তির মত, যাদের নেহাৎ কৃপাবশে কেউ দুটো আতপ এক মুঠো বেলপাতা এক কুশি গঙ্গাজল দিয়ে যায়।
এক বছরের উপর আমি ইংল্যান্ডে ছিলাম। ফিরে এসে ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াচ্ছি জমিদার এবং অভিজাত বংশের যোগ্য একটি জীবনধারার জন্য, তার জন্য বাঈজীপাড়া থেকে শুরু ক’রে হোটেল, বার, সাংস্কৃতিক শিল্পী-জীবনের নানা কর্নার খুঁজে বেড়াচ্ছি; অজস্র অর্থব্যয় করছি-এর মধ্যে জানবাজারের নায়েব আচার্যির পত্র পেয়েছি—“এরূপ অর্থব্যয় করিলে আর বৎসরখানেকের মধ্যেই সঞ্চিত অর্থ ব্যয়িত হইয়া দেনাগ্রস্ত হইবেন। আপনার এইরূপ ব্যয় অন্য দিকে জমিদারী একরূপ দায় ও বোঝার মত হইয়া উঠিয়াছে। কীর্তিহাটের কাছারীর সংবাদ এই যে, গত বৎসরের মধ্যে জমিদারীতে একরূপ খাজনা আদায়ই হয় নাই। শুধু আমাদেরই নয়; সকলেরই এক দৃশ্য। অধিকাংশ জমিদারকেই দেনা করিয়া কালেক্টারী রেভেন্যু দাখিল করিতে হইয়াছে। গত বৎসর আমাদের সঞ্চিত তহবিল হইতে কালেক্টারী ও পত্তনী খাজনা দাখিল করিতে কুড়ি হাজার টাকার কিছু বেশী দিতে হইয়াছে। এবং তামাদির মুখে বাকী খাজনার নালিশ করিতে রশুম খরচ দিতে হইয়াছে আট হাজার টাকা। এ টাকা কতদিনে আদায় হইবে তাহার স্থিরতা নাই। আপনি এইরূপভাবে দেশান্তরে বিপুল অর্থব্যয় করিয়া ঘুরিয়া না বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিয়া সরেজমিনে সমস্ত দেখিয়া বুঝিয়া একটি নির্দিষ্ট পথে চলিবার ব্যবস্থা করুন। এদিকে যুদ্ধ বাধিয়াছে। অনেকে অনেক রকম বলিতেছে। আপনি সত্বর আসিয়া কার্যভার স্বহস্তে লইলে ভাল হয়।”
চিঠিখানা বৃন্দাবনে আসবার দিন পনের আগে পেয়েছিলাম। এবং ভেবেছিলাম ফিরে গিয়ে জমিদারী বিক্রি করে দিয়ে জীবনের সঙ্গে বংশের ইতিহাসের সম্পর্কটা ঘুচিয়ে দেব। কিন্তু সেদিন মৃত্যুশয্যায় ঠাকুমা দেবেশ্বর রায়ের লাঞ্ছিতা গৃহিণী আমার পিতার গর্ভধারিণীর কাছে প্রতিশ্রুতি দিলাম—না, জমিদারী বেচব না। রাখব—রাখবার চেষ্টা করব জমিদারী।
সত্যিই তো, কীর্তিহাটের লোকে দেখে যদি নমস্কার না করে কীর্তিহাটে ঢুকব কি করে?
হঠাৎ হেসে ফেলে সুরেশ্বর বললে—কিছু মনে করো না সুলতা, তুমি পলিটিক্স কর—বল তো, একবার মিনিস্টার হয়ে দেশের লোকের সেলাম নমস্কার কুড়িয়ে তারপর কি আর মিনিস্টার না হয়ে লোকের কাছে বের হওয়া যায়!
সুলতা ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে ছোট রুমালখানা বের করে চোখ মুছে বললে—তোমার ঠাকুমার কথা বল। রাজলক্ষ্মী আর ভোটলক্ষ্মীতে এক করে গণ্ডগোল করো না, পাকা সোনা আর গিল্টি এক নয়।
সুরেশ্বর বিষণ্ণ হেসে বললে—ঠাকুমার কথা তোমার ভাল লেগেছে সুলতা?
—প্রশ্নটা নাই বা করলে সুরেশ্বর। তিনি সত্যিই বাংলাদেশের জমিদারলক্ষ্মীর সিম্বল। বাংলাদেশের জমিদারেরা এই লক্ষ্মীর অঙ্গের অলঙ্কার কেড়ে নিয়ে বাঈজী পুষেছে, জুয়া খেলেছে, এই মাটির ছেলেদের ঘাড়ে বাপ-ছেলে-সম্পর্ক চাপিয়ে তাদের গোলাম করেছে। বল—তাঁর কথা বল।
সুরেশ্বর বললে—তিনি আর এক দিন বেঁচেছিলেন এই কথাবার্তার পর। মৃত্যু হল ভোররাত্রে। সকালবেলা হঠাৎ বললেন—নাতি, তুই বিয়ে করবি নে?
বেশ ভাল সেদিন। সকালবেলা উঠে ইষ্ট স্মরণ করে মধু দিয়ে মকরধ্বজ খেয়ে গুনগুন করে নাম করছিলেন, আমি গিয়ে বসলাম। আমাকে হঠাৎ প্রশ্নটা করলেন।
মেজদি ওষুধ খাওয়াচ্ছিলেন, তিনি বললেন—আপনি বলুন দিদি। বাপ-মা চলে গেছেন, একমাত্র তুমিই বলতে পার—বাধ্য করতে পার। বল তুমি।
—বিয়ে কর ভাই।
অর্চনা বলে উঠল—আমি ভেবেছিলাম ঠাকুমা, বিলেত গেল সুরোদা, মেমসাহেব বিয়ে করে ফিরছে। ওমা কোথায়?
—তা করলি নে কেন রে সুরেশ্বর?
হেসে বললাম—তোমার জন্যেই করি নি ঠাকুমা।
—কেন?
—তা হ’লে কি আমার হাতের শ্রাদ্ধের নৈবেদ্য তুমি খুশী মনে নিতে? নিতে পারতে?
—নিতাম। নিশ্চয় নিতাম। বিয়েতে জাত মানতে নেই রে। তুই বিয়ে কর, দেখ তার সেবা তার হাতে জল আমি খাই কিনা।
সন্ধ্যেবেলা বললেন—কথাটা ডেকে বললেন-সুরেশ্বর, আমার শ্রাদ্ধ তুই করবি তো? যজ্ঞেশ্বর করবে না। সে এলো না। আমার ভিক্ষেশাশুড়ীর আশ্রমে আছি কিনা, তাই করবে না। তুই করবি?
চোখে আমার জল এল। বললাম- আমি যে তারই জন্যে ছুটে এসেছি ঠাকমা।
একটু চুপ করে থেকে বললেন—দেখ, মেজঠাকুরপোর ছেলেরা আমাকে গোবিন্দের চত্বরে ঢুকতে দেয় নি। আমি সেই রাত্রে গোয়ানপাড়া গিয়েছিলাম, গির্জের পাদরীর কাছে, ভায়লার শ্রাদ্ধের জন্য টাকা দিতে। সেখানে জল খেয়েছিলাম। বড়বাবুর মৃত্যুর পর আমি মরতে পারি নি, সঙ্গে যেতে পারি নি, কিন্তু ভায়লা পেরেছিল, সে বিষ খেয়ে মরেছিল। সেইজন্যে আমার ইচ্ছে ছিল—বড়বাবুর শ্রাদ্ধ হল, ভায়লার শ্রাদ্ধ করুক ওরা। তা টাকা ওরা নেয় নি। এদিকে এরা আমাকে পতিত বলে মন্দিরে ঢুকতে দিলে না। যজ্ঞেশ্বর পাগল বলে আমাকে ঘরে বন্ধ করে রাখলে। আমার কোম্পানীর কাগজ কেড়ে নিলে। মনে দুঃখ খুব পেয়েছিলাম, তাই পালিয়ে এসেছিলাম বৃন্দাবন। তা আমার বেশী ধুমধাম করে শ্রাদ্ধ করবি ভাই, ওই কীর্তিহাটে গোবিন্দের নাটমন্দিরে, দানসাগরটাগর নয়—চারটে ষোড়শ করে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ।
বললাম—করব ঠাকুমা।
তিনি বললেন—“সেই তুষ্টিরাম বামুনদের আনাস যেন। বুঝলি! চাবি দিয়ে ঘটি বাজিয়ে গান গাইবে—’ওগো সুরেশবাবু গো, শ্রবণ কর, তুমি শ্রবণ কর গো। তোমার পুণ্যবতী পিতামহী উমাদেবী বৃন্দাবনে গোবিন্দের রাঙা চরণতলে তাঁর মুখারবিন্দ দেখতে দেখতে দেহত্যাগ করলেন, তারপর ধীরে ধীরে যমুনায় গিয়ে স্নান করে দিব্য নববস্ত্র পরিধান করলেন, ললাটে নাসিকায় তিলক আঁকলেন, বক্ষস্থলে রাধা-গোবিন্দ নাম লিখলেন এবং গোবিন্দমন্দিরে রাধা-গোবিন্দকে দর্শন করে বাহিরে এলেন, সেখানে মকরকেতনে রতিপতির মত দিব্য মনোহরকান্তি তোমার পিতামহ, বড় রায় মহাশয় সমাদর করে বললেন–এস, এস, এস আমার প্রিয়তমা প্রাণেশ্বরী, আমি তোমাকে স্বর্গধাম থেকে নিতে এসেছি-এস—”
বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল সুলতা, দু চোখে ধারা বেয়ে নামতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও কেঁদেছিলাম। মেজদি কেঁদেছিলেন হা-হা করে। অর্চনা কেঁদেছিল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তাঁর জীবনের সমস্ত অবরুদ্ধ বাসনা অতৃপ্ত কল্পনা সেদিন শ্রাবণের বর্ষণের মত ঝরঝর ধারায় যেন ঝরে পড়েছিল আমাদের সবারই চোখের জলের ধারায়। কিন্তু যখন মারা গেলেন তখন একটি কথাও বললেন না। কাউকে ডাকলেন না। আমরা কেউ জানতেই পারলাম না; শুধু সকালে উঠে অর্চনা এবং মেজঠাকুমা দেখলেন, ঠাকুমা নেই, তিনি চলে গেছেন।
রায়বংশের ইতিহাস এবার মোহনার মুখে নদীর অবস্থার মত। গোটা জাতটার জীবনে তখন জোয়ার এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে রায়বংশের জীবনস্রোতের মুখে বালির চড়া ঠেলে দিয়েছে; গতি রুদ্ধ হয়ে গেছে; কোনক্রমে শতধারা হয়ে নালার মত ধারায় দু’-চারটে স্রোত গিয়ে পড়ছে। বাকি সব মজা বিলের মতো কাদায়-জলে থক থক করছে।
সুতরাং জবানবন্দী এখানেই শেষ হত। আমি সঙ্কল্পমত জমিদারী বিক্রী করে দিয়ে রায়দের বংশতালিকা হতে স্বচ্ছন্দে নাম কাটিয়ে নিজেকে হারিয়ে দিতে পারতাম। সম্পত্তি বিক্রি না করলে রায়বাড়ীর কৃতকর্মের জের থেকে রেহাই নেই। একটা বিচিত্র কথা বলি, সংসারে ধর্মান্তর গ্রহণ করলে বা জাত ফেলে দিয়ে বংশতালিকা থেকে নাম কাটিয়েও রেহাই মেলে না, সম্পত্তির অংশীদার হিসেবে শরিকদের দায় ঘাড়ে চাপে। কিন্তু সম্পত্তি বিক্রী করে দিলেই তুমি খালাস। সে খালাস আমার আর হল না; হল না ঠাকুমার জন্যে। তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিলাম, সম্পত্তি বেচব না। অবিশ্যি তাঁকে কথা না দিলেও আমি বেচতে পারতাম কিনা সন্দেহ। আজও মনে হচ্ছে বিক্রী করাই উচিত ছিল, কিন্তু বেচতে বোধ হয় পারতাম না। সম্পত্তির মমতায় যে-কথা ঠাকুমা বলেছিলেন, সেটা মিথ্যে নয়। ভূমির মত সম্পত্তি নেই। ভূমির উপর অধিকার কায়েম করতে পারলে গাছপালা, ফলফুল, জীবজন্তু থেকে মানুষ পর্যন্ত তার সম্পত্তি হয়।
কথাটা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলাম কীর্তিহাটে ফিরে এসে। না, যা ভাবছ তা নয়। প্রজারা সম্বর্ধনা করে নি, তারা গ্রাহ্যই করে নি বলতে গেলে, শরিক অর্থাৎ রায়বাড়ীর মেজতরফের যাঁরা তখনও সক্রিয়, তাঁরা বিরক্ত হলেন, বিদ্বিষ্ট হলেন, এ আপদ আবার কোত্থেকে এল। গ্রামের প্রধান এবং নায়ক তখন কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট। মানুষেরা তাঁকেই মানে। জমিদারের বিরুদ্ধে একটা উদ্ধত মনোভাব, গর্তের সাপের মত অহরহ উত্তপ্ত নিঃশ্বাসের মত অনুভব করা যায়। তবু ভাল লাগল। রায়বাড়ীর ইট-কাঠ, বাড়ীঘর, পুকুর বাঁধাঘাট, গাছপালা, ক্ষেতখামার—নদীর ওপারে সিদ্ধাসন, জঙ্গলের ওপাশে গোয়ানপাড়া, সবাই যেন মনকে ভরে দিলে। যেন আমাকে জড়িয়ে ধরলে।
শতজনের বিমুখতা এবং অপ্রসন্নতা আমাকে অথবা কীর্তিহাটের প্রকৃতিকে বা রায়বাড়ীকে অপ্রসন্ন করতে পারে নি; অন্তত আমার চোখে দোল খাওয়া গাছপালা, পাখীর ডাক আমার কানের কাছে বার বার বলেছিল, আমরা তোমার, আমরা তোমার। আমার মন বলেছিল—এসব আমার, এসব আমার!
ঠাকুমা মারা গিয়েছিলেন অগ্রহায়ণ মাসে; প্রথম দশদিনে একটা তিলকাঞ্চন শ্রাদ্ধ বৃন্দাবনে করেছিলাম। টেলিগ্রামে জ্যাঠামশাইকে খবর দিয়েছিলাম; কীর্তিহাটে খবর দিয়েছিলাম। প্রথম শ্রাদ্ধ শেষ করে অর্চনা এবং মেজদিকে নিয়ে কলকাতা ফিরেছিলাম। কলকাতায় মাস দুয়েক থেকে ফাল্গুনের প্রথমে কীর্তিহাটে এলাম। এলাম ওই ঠাকুরমাকে দেওয়া আমার কথা রাখবার জন্য। ওখানে গোবিন্দমন্দিরের চত্বরে, যে চত্বরে মেজতরফের ধনেশ্বর রায় এবং জগদীশ্বর রায় ঠাকুমাকে ঢুকতে দেয় নি, সেই চত্বরে ঘটা করে একটি শ্রাদ্ধ আমি করব। বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ। চারটি ষোড়শ করব, তার মধ্যে একটি রূপোর। এই সব কল্পনা করে কীর্তিহাটে ফিরলাম। নায়েবকে লিখেছিলাম, এখন হয়তো কিছুদিন থাকব ওখানে। সুতরাং ওখানকার বাড়ীঘর মেরামত করবার ব্যবস্থা করবেন এবং বাড়ীর ভিতরটা সবই চুনকাম এবং বাইরেটা রঙ ফেরাবেন। শরিকেরা যদি তাঁদের অংশে রঙ ও চুনকাম করতে বাধা দেন, তবে তাঁদের অংশ বাদ দিয়ে আমার অংশই করাবেন।
অনুমান করেছিলাম, বাধা কেউ দেবে না। সে অনুমান ষোল আনার মধ্যে একের ছয় মিথ্যে হয়েছিল, বাকী পাঁচের ছয় ভাগ হয়েছিল সত্যি; এক ধনেশ্বরকাকা ছাড়া বাকী সকলেই মত দিয়েছিলেন। শুধু ধনেশ্বরকাকা বলেছিলেন, না। আমার অংশ বাদ দিও। রঙের পোঁচড়া আমার অংশে যেন না ঠেকে।
হয়তো জগদীশ্বরকাকা থাকলেও ওঁর সঙ্গে সায় দিতেন; কারণ ঠাকুমার দরজা আটকাতে দুই ভাই দাঁড়িয়েছিলেন এবং ধনেশ্বরকাকাই বলেছিলেন অপ্রিয় কথাগুলি। সে-কথা ধনেশ্বরকাকা ভুলতে পারেন নি। এবং আমার টেলিগ্রাম যখন ঠাকুমার মৃত্যুসংবাদ নিয়ে এখানে তাঁর কাছেই পৌঁছেছিল তখন তিনি বলেছিলেন, না, অশৌচ নেব না। নিতে আমি পারি না। কিন্তু নিতে তাঁকে হয়েছিল গোবরডাঙার খুড়ীমার নির্দেশে এবং আরও একজন এ নির্দেশ দিয়েছিল, সে হল অতুলেশ্বর। অতুলেশ্বর সদ্য জেল থেকে বেরিয়েছে। গোবরডাঙার খুড়ীমা বলেছিলেন—বাতে পঙ্গু হয়েছ, এবার মুখ থেকে পোকা পড়বে ও কথা বললে। কোন মুখে বলছ এ কথা? অশৌচ নেবে না?
অশৌচ তিনি নিয়েছিলেন, কিন্তু বাড়ী মেরামতের চুনকামের প্রস্তাবে তাঁকে কেউ নড়াতে পারে নি। গোবরডাঙার খুড়ীমা অনেক অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু ধনেশ্বরকাকা কিছুতে রাজী হন নি। না, তা আমি পারব না, এই হয়েছিল তাঁর বুলি, তখন তিনি ব্যাধিতে শয্যাশায়ী। যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি বাত। বাতে তিনি তখন পঙ্গু। যৌবনের দুরারোগ্য যৌনব্যাধির পরিণাম।
মনে মনে দুঃখ পেয়েছিলাম। পেয়েছিলাম এই জন্যে যে, ওঁরা যাই করে থাকুন, আমি আজও পর্যন্ত তো ওঁদের সঙ্গে কোন বিরোধ করি নি। তবে কেন প্রত্যাখ্যান করলেন! ঠকিয়ে বা জবরদস্তি করেও তো অনেক কিছু নিয়েছেন আমার, তবে যখন আমি উপযাচক হয়ে তাঁর অংশের বাড়ী মেরামত করাতে চাইলাম, তখন না বললেন কেন? সঙ্গে সঙ্গে আবার ভালও লেগেছিল। তিলকাঞ্চন শ্রাদ্ধের এক কুচি সোনার মতই ভাল লেগেছিল।
* * *