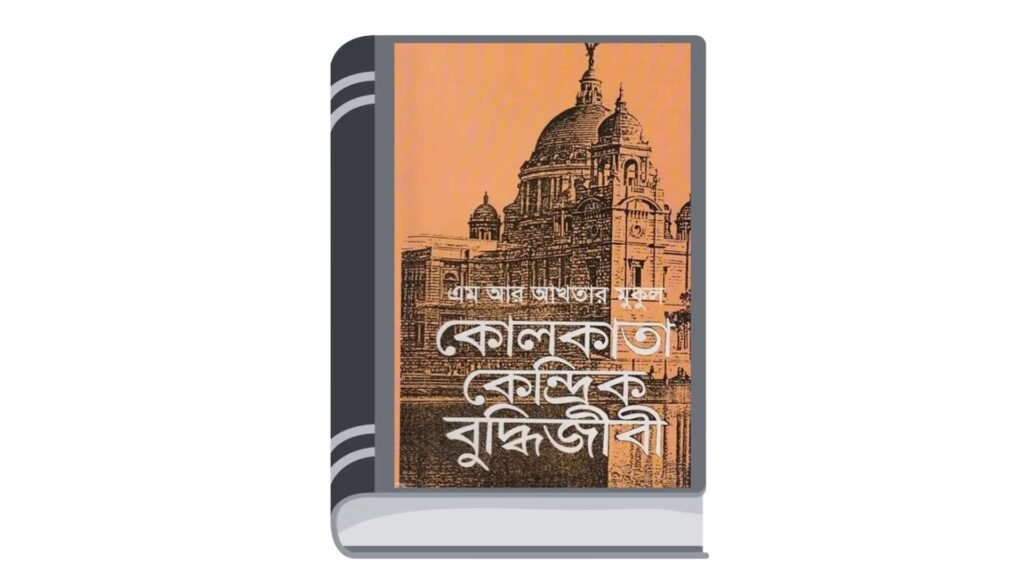কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী – ১৩
বঙ্গভঙ্গ ও রবীন্দ্রনাথ
নানা চাঞ্চল্যকর ঘটনা-প্রবাহের ফলশুরতিতে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত মোট ৯৮ বছর সময়কালকে উপমহাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। একথা চিন্তা করলে আজ বিস্ময়কর মনে হয় যে, ইংরেজরা এদেশে আগমনের পর কোলকাতাকে কেন্দ্র করে ইংরেজদের সমর্থকগোষ্ঠী হিসেবে যে বাঙালি বৰ্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়েছিলো, তাঁরা মনে আঘাতপ্রাপ্ত হবে বিবেচনা করে বৃটিশ পার্লামেন্টে একটা অর্থবহ আইন পাশ করা হয়েছিলো। এই আইনে বলা হয়েছিলো যে, ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংরেজ ভারতে খ্রীষ্টান মিশনারীরা তাঁদের খৃষ্ট ধর্ম প্রচার করতে পারবে না এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ছাড়া আর কোন ইংরেজ কোম্পানীর ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্য করার অধিকার থাকবে না। এর পরবর্তীতে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে একদিকে দুই দফায় কট্টর শরিয়তপন্থীদের ওয়াবী আন্দোলন ও সিপাহী বিপ্লব এবং অন্যদিকে উদার ও সংস্কারপন্থী রামমোহন ইয়ং বেংগল-মাইকেল-বিদ্যাসাগর প্রমুখের কর্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয়।
১৮৭১-এর পরবর্তীতে হিন্দু জাতীয়তাবাদের পুনর্জাগরণ
কিন্তু ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ঘটনাপ্রবাহ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে শুরু করে। এ বছর কোলকাতায় মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরীর ঐতিহাসিক ফতোয়ার জের হিসেবে উত্তর ভারতীয় এবং বংগীয় এলাকার মুসলিম মধ্যবিত্তরা যখন এদেশে ইংরেজ শাসনকে মেনে নিয়ে ইংরেজী শিক্ষায় মনোনিবেশ করে, ঠিক তখনই হিন্দু ধর্ম, হিন্দু বাহুবল এবং হিন্দু শৌর্যবীর্যের জয়গান করে একে একে আবির্ভার হলো বংকিম রামকৃষ্ণ-দয়ানন্দ-বিবেকানন্দ-অরবিন্দর মতো মণীষীদের। উদার ও সংস্কারপন্থীদের কর্মকাণ্ডগুলোর হয় বিস্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে গেলো, না হয় এসবের ভ্রমাত্মক ব্যাখ্যা দান করা হলো। পশ্চিম বংগের প্রখ্যাত গবেষক ডঃ অরবিন্দু পোদ্দারের মতে,
“…… বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয়তাবাদকে একটা ধর্মীয়-আধ্যাত্মিক আলোকে মণ্ডিত করেন। ভারতবর্ষ নামক যে একটি ভৌগোলিক সত্তা, তাকে তিনি মাতৃরূপে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন, এই মাতৃভাবনা স্বর্গীয় দেবী-ভাবনার সমতুল্য। ‘বন্দেমাতরম’ সংগীতে (স্বাধীন ভারতের জাতীয় সংগীত নয়) তিনি দেশজননীকে দুর্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সংগে একাত্ম বলে বর্ণনা করেছেন। অন্য কথায়, হিন্দু রাজত্ব স্থাপন এবং তারই অনুপ্রেরণায় ভবিষ্যৎ ভারতকে নির্মাণ করার আদর্শ তিনি (শ্রীঅরবিন্দু) প্রচার করেছিলেন। হিন্দু ঐতিহ্য আশ্রিত সমস্ত লেখকের দৃষ্টিতেই……. সৃজনধর্মী ও বুদ্ধিমার্গীয় উভয়তঃ ….শ্রীকৃষ্ণই হলেন একমাত্র পুরুষ যিনি বর্তমানের পরাধীন ও শত লাঞ্ছনায় ছিন্নভিন্ন ভারতবর্ষকে এক শক্তিশালী প্রগতিশীল দুর্জয় সত্তায় রূপান্তরিত করতে পারেন।……….. তাঁদের (নেতৃবৃন্দের) সুদূর বিশ্বাস কেবলমাত্র হিন্দু দার্শনিক চিন্তা, জীবনদর্শন এবং এর সংশেষবাদী ধর্ম দ্বারাই অতীতে এই বিরাট ভূখণ্ড ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ঐক্য অর্জিত ও সুরক্ষিত হয়েছিল এবং ভবিষ্যতেও পুনরায় সেই আদর্শের শক্তিতেই নবভারতের আবির্ভাব ঘটবে।” (রবীন্দ্রনাথ/রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ১৯৮২ ‘উচ্চারণ’ কলিকাতা)।
এ ধরনের এক প্রেক্ষাপটে স্বল্পদিনের ব্যবধানে বাংলা সাহিত্যের গৌরব রবীন্দ্র প্রতিভার আবির্ভাব হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে এই প্রতিভা কিভাবে আপন মহিমায় বিকশিত হয়ে উঠে সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম কোলকাতার অন্যতম বনেদী জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে। গবেষক বিনয়ঘোষ বাংলার নবজাগৃতি পুস্তকে (প্রকাশক : ওরিয়েন্ট লংম্যান : ২য় সংঃ আষাঢ় ১৩৯১ : কলিকাতা : পূঃ ৫৯-৬০) এ সম্পর্কে বলেছেন, “বহু বিস্তৃত সমৃদ্ধশালী ঠাকুর পরিবারের প্রধান শাখার আদি পুরুষ দর্পনারায়ণ ঠাকুর হুইলার সাহেবের দেওয়ানী করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন।” পরবর্তীকালে এই পরিবারের দ্বারকা নাথ ঠাকুর ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে অবিভক্ত বাংলার অন্যতম ধনাঢ্য ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন কোলকাতা কেন্দ্রিক হিন্দু বাঙালি বিত্তশালীদের অগ্রণী। বিদেশে নীল ও রেশম রফতানী ব্যবসায় দ্বারকানাথের কর্মদক্ষতা এবং পরবর্তীতে ইউনিয়ন ব্যাংক-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হওয়া ছাড়াও তাঁর শিল্পোদ্যোগ লক্ষ্য করে ইংরেজরা পর্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছিলো (ফিসার্স কলোনিয়াল ম্যাগাজিন : ১৮৪২: পৃঃ ৩৯৪-৩৯৫)।
এই দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঔরসে উপমহাদেশের গৌরব এবং এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম হয়। রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে তৎকালীন কোলকাতা নগরীর একটা পরিচ্ছন্ন চিত্র পাওয়া যায়। ‘ছেলেবেলা’ পুস্তকে তিনি লিখেছেন “…… তখন কাজের এত বেশী হীস-ফাসানী ছিল না, রয়ে বসে দিন চলত। বাবুরা অফিসে যেতেন কষে তামাক টেনে নিয়ে পান চিবতে চিবতে, কেউ বা পালকি চড়ে, কেউ বা ভাগের গাড়ীতে যারা ছিলেন টাকাওয়ালা তাঁদের গাড়ি ছিল তকমা আটা, চামড়ার আধঘোষটাওয়ালা, কোচবাক্সে কোচম্যান বসত মাথায় পাগড়ি হেলিয়ে, দুই দুই সইস থাকত পিছনে, চামরবাধা, হেঁইয়ো শব্দে চমক লাগিয়ে দিত পায়ে চলতি মানুষকে। মেয়েদের বাইরে যাওয়া-আসা ছিল দরজাবন্ধ পালকির হাঁপ ধরানো অন্ধকার, গাড়ি চড়তে ছিল ভারি লজ্জা।”
এহেন রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কোলকাতা কেন্দ্রিক হিন্দু বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভিত্তি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে শাসক ইংরেজ রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা লাভের প্রত্যাশায় ১৮৬৭ সালে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠিত হয়।
এই হিন্দু মেলার প্রথম অধিবেশনে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত গান
“মিলে সব ভারত সন্তান,
একতান মনঃপ্রাণ
গাও ভারতের যশোগান”
এবং গগণন্দ্রেনাথ ঠাকুরের রচিত “লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে……” গান পরিবেশিত হয়। হিন্দুমেলায় প্রথম অধিবেশনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘উদ্বোধন’ শিরোনামে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। প্রথম দু’টি লাইন হচ্ছেঃ
“জাগ জাগ সবে ভারত সন্তান।
মাকে ভুলি কতকাল রহিবে শয়ান?”
এখানে বিশেষ করে বলতে হয় যে, আলোচ্য সময়ে জোড়াসাঁকোর এই ঠাকুর পরিবারে হিন্দুমেলাকে কেন্দ্র করে তুমুল উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল এবং পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ প্রায় সবাই কোন না কোনভাবে হিন্দুমেলার সংগে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ তাঁর শৈশব কাল থেকে এ ধরনের ভাবধারার সংগে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। এমনকি তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘সঞ্জীবনী সভা’রও অন্যতম সদস্য ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি স্বয়ং এ সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেছেন। “কলিকাতার এক গলির মধ্যে এক পোড়াবাড়ীতে সেই সভা বসিত। সেই সভার সমস্ত অনুষ্ঠানই রহস্যে আবৃত ছিল। বস্তুতঃ, তাহার মধ্যে ওই গোপনীয়তাটাই একমাত্র ভয়ংকর ছিল। ………..দ্বার আমাদের রুদ্ধ, ঘর আমাদের অন্ধকার, দীক্ষা আমাদের ঋকমন্ত্রে, কথা আমাদের চুপিচুপি— ইহাতেই সকলের রোমহর্ষণ হইত, আর বেশী কিছুই প্রয়োজন ছিল না। আমার মতো অর্বাচীনও এই ভ্রাতার সভ্য ছিল। সেই সভায় আমরা এমন এক খ্যাপামির তপ্ত হাওয়ার মধ্যে ছিলাম, যে অহরহ উৎসাহে যেন উড়িয়া চলিতাম।……….. এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ উত্তেজনায় আগুন পোহানো” (জীবনস্মৃতি : রচনাবলী ১০ম পৃঃ ৬৭)
গবেষক ডঃ প্রভাত কুমার গোস্বামীর ভাষায় বলতে গেলে, “এই উত্তেজনার আগুন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখ নাট্যকারদের নাটককে স্পর্শ করেছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাটককে স্পর্শ করেনি। ………. রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম পুর্নবয়ব নাটক রাজা ও রানীতে (১৮৮৯) রাজা আছেন, রানী আছেন, মন্ত্ৰী আছেন… কিন্তু তারা ইতিহাসের কেউ নন। ……….এর মধ্যে গ্রথিত তথ্য ও তত্ত্ব কোনটাই ঐতিহাসিক নয়। কিন্তু তথাপি নাটকটিতে বিদেশী শাসনের প্রতি বারবার কটাক্ষ থাকায় ইংরেজ সমালোচক এডওয়ার্ড থমসন এর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার আভাষ পেয়েছেন।”
রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘বৌঠাকুরানীর হাট ১৮৮১ সালে রচনা করলেও (‘ভারতী পত্রিকায় ১২৮৮-এর অগ্রহায়ণ থেকে ১১টি সংখ্যায় প্রকাশিত) ১৮৮৩ সালে তা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তিনি ‘প্রায়চিত্ত’ নামে এর নাট্যরূপ দেন ১৯০৯ সালে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটিকা ‘রুদ্রচণ্ড’ (১৮৮১) হওয়া সত্ত্বেও সমালোচকদের মতে এটা হচ্ছে “গাঁথা কাব্য” তাই সত্যিকারভাবে বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক রচনা শুরু হয় ঊনবিশং শতাব্দীর নবম দশক থেকে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এ ধরনের একটা পারিবারিক পরিবেশ এবং তৎকালীন কোলকাতার বর্ণ হিন্দু বাঙালিত্বের ধুলিঝড়ের মাঝে থেকেও তিনি কেমন করে ‘রাজা ও রানী’ নাটকে মুক্তবুদ্ধি মনমানসিকতার পরিচয় দিতে সক্ষম হলেন? তিনি কেমন করে এই রূপক নাটকে মূল শত্রু বিদেশী পরাশক্তিকে চিহ্নিত করে কটাক্ষ করলেন? এর জবাবে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, এটাই ছিলো হিমাচল সদৃশ রবীন্দ্র-প্রতিভার উন্মেষের যুগ। মাত্র ১২ বছর বয়স থেকে ৮০ বছর পর্যন্ত রবীন্দরনাথ অবিশ্রান্তভাবে কবিতা, গান, উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখে গেছেন। ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রথম কবিতা ‘অভিনাষ’।
এখানে লক্ষণীয় যে, জ্যেষ্ঠা ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নির্দেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দুমেলায় নবম অধিবেশনে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। কিন্তু কবিতাটির কোথাও সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি কটাক্ষ কিংবা হিন্দু বাহুবল ও বীর্যবত্তার অহেতুক গুণকীর্তণ নাই। কবিতাটিতে তিনি কেবলমাত্র দেশ-বন্দনা করেছেন। কবিতার অংশবিশেষ নিম্নরূপঃ
“ভারত কঙ্কাল আর কি কখন,
গাইবে হায়রে নতুন জীবন,
ভারতের ভষ্মে আগুন জ্বালিয়া
আর কি কখন দিবে সে জ্যোতি।”
অথচ এরই পাশাপাশি বাংলা গদ্য সাহিত্যের অন্যতম স্তম্ভ ঔপনাসিক বংকিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়-এর অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর ‘রাজসিংহ’ উপন্যাস-এর প্রতি আলোকপাত করা সমীচীন হবে। অবশ্য এর আগেই বংকিম-এর ‘দুর্গেশনন্দিনী’ (১৮৬৫) প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৮২ সালে বংকিমচন্দ্র ‘রাজসিংহ’ উপন্যাসটি রচনা করেন। কিছুদিনের মধ্যে এই উপন্যাস-এর তিনটি ক্ষুদ্রাকৃতি সংস্করণ নিঃশেষিত হলে ১৮৯৩ সালে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে রাজসিংহ উপন্যাস-এর ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বংকিমচন্দ্র এই ৪র্থ সংস্করণের ভূমিকায় লিখলেন, “ইংরেজ সাম্রাজ্যে হিন্দুর বাহুবল লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তারা পূর্বে কখনও লুপ্ত হয় নাই। হিন্দুদিগের বাহুবলই আমার প্রতিবাদ্য। উদাহরণ স্বরূপ আমি ‘রাজসিংহ’ লইয়াছি।”
এই ‘রাজসিংহ’ গ্রন্থেই বংকিমচন্দ্র সরাসরিভাবে মোগল সম্রাট আওরংগজেব-কে “ধূর্ত, কপটাচারী, পাপে সঙ্কোচশূন্য, স্বার্থপর, পরশীড়ক” প্রভৃতি বিশেষণে আখ্যায়িত করেছেন। এতে করে স্বাভাবিকভাবেই এই ভারতভূমিতে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী সম্প্রদায় বিশেষের মন আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে বলা যায়। উপরন্তু বংকিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসগুলোতে প্রায়শইঃ সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করে ভেবেছিলেন তিনি ‘হিন্দুবাহুবল’-এর পক্ষে সোচ্চার এবং বাঙালি তথা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার ‘মহান ব্রতে’ লিপ্ত হয়েছেন।
১৮৮২ সালে বংকিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার পর ১৮৮৩ সালেই শ্ৰী কেদার চৌধুরী এর নাট্যরূপ দান করে কোলকাতার ন্যাশনাল থিয়েটারে মঞ্চস্থ হলে একথা পরিস্ফুট হয় যে, বংকিম প্রতিভা সাম্প্রদায়িক কেদাক্ত আবর্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। ইতিহাস সাক্ষী দেয় যে, তাঁর চিন্তাধারা অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে সংকীর্ণ ও বিপথগামী ছিলো।
এক্ষণে আমরা আলোচনার সুবিধার্থে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে অবিভক্ত বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সম্পর্কে আরও কিছুটা আলোকপাত করা বাঞ্ছনীয় মনে করছি। কোলকাতার যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে তাঁর জন্ম, সেই ঠাকুর পরিবার কয়েক পুরুষ ধরে পরাশক্তি ইংরেজদের বদৌলতে সমৃদ্ধির সোপান বেয়ে ঊর্ধ্বমুখে ধাবিত। রবীন্দ্রনাথ যখন কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করছেন তখন কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদী পৃষ্ঠপোষকতার একটা সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এর নেতৃস্থানীয়রা তখন ইউরোপীয় রেনেসাঁর অনুকরণে বাঙালার নব জাগৃতির দাবীদার এবং ‘হিন্দু রিভাইভালিজম’-এর লক্ষ্যে একটা সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের চৌহদ্দি খুঁজে বেড়াচ্ছেন।
কৈশোরের প্রান্তসীমায় এসে রবীন্দ্রনাথ মর্মে মর্মে অনুভব করলেন যে, স্বীয় অগ্রজ এবং সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান ‘হিন্দুমেলার’ অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে ব্যক্তিত্বের প্রভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধার প্রচেষ্টা করছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একাধারে হিন্দু সমাজ-সংস্কার ও প্রখ্যাত নাট্যকার হিসাবে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর পুরোধা এবং অন্যদিকে উদীয়মান রাজনীতিবিদ ও হিন্দু রিভাইভালিজম’-এর প্রবক্তা।
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রবীন্দ্র-কাব্যের ‘বৃটিশ’ শব্দ বদল করে ‘মোগল’ বসালেন
তাই একথা অনুধাবন করা সংগত হবে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রবীন্দ্রনাথকে নীরবে বহু বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়েছে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বীয় রচিত সাম্প্রদায়িক নাটকগুলোতে রবীন্দ্রনাথের কবিতার যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর রচিত ‘পুরুবিক্রম’ নাটকের দ্বিতীয় সংস্করতা (১৮৭২) রবীন্দ্রনাথের ‘এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্ত্রটি মন’ গান, ‘সরোজিনী’ (১৮৭৫) নাটকের শেষ অংকে “জ্বল, জ্বল, চিতা। দ্বিগুণ, পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা।” গান এবং ‘স্বপ্নময়ী’ (১৮৮২) নাটকে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজবিরোধী একটি কবিতাকে বদলিয়ে ব্যবহার করেছেন। ১৮৭৬ সালে বৃটিশ পার্লামেন্টের একটি আইন অনুসারে মহারানী ভিক্টোরিয়াকে ‘ভারত সম্রাজ্ঞী’ উপাধি দেয়া হলে ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড লিটন মহাসমারোহে দিল্লীতে দরবার বসিয়ে মহারানী ভিক্টোরিয়াকে ভারতের সম্রাজ্ঞী বলে ঘোষণা করেন। ১৮৭৬ সালেই লর্ড লিটন ‘নাটক নিয়ন্ত্রণ আইন’, ‘অস্ত্ৰ আইন’ এবং ‘ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্ট’ প্রবর্তন করেন। ফলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দিল্লীর দরবারকে উপলক্ষ করে একটা চমৎকার ইংরেজবিরোধী কবিতা রচনা করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৮২ সালে তাঁর রচিত চরম সাম্প্রদায়িক ‘স্বপ্নময়ী’ নাটকে এই কবিতাটি শুভ সিংহের কণ্ঠে ব্যবহার করলেন।
আলোচ্য কবিতার কয়েকটি পংক্তি নিম্নরূপঃ
“তোমারে শুধাই হিমালয়গিরি,
ভারতে আজি কি সুখের দিন?
তবে এই সব দাসের দাসেরা,
কিসের হরষে গাইছে গান? …..
ব্রিটিশ বিজয় করিয়া ঘোষণা,
যে গায় গাক্ আমরা গাব না
আমরা গাব না হরষ গান,
এস গো আমরা যে ক-জন আছি,
আমরা ধরিব আরেক তান।”
রবীন্দ্রনাথের এই কবিতায় যেসব জায়গায় “বৃটিশ” শব্দ ছিল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেসব জায়গায় দিব্বি “মোগল” শব্দ বসিয়ে স্বীয় সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করলেন। পশ্চিম বাংলার গবষেক শ্রী প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়-এর মতে, “রবীন্দ্রনাথের দিল্লীর দরবারের বিরুদ্ধে লিখিত কবিতা অদলবদল করিয়া আশ্রয় পাইল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বপ্নময়ী নাটক।” (ভারতে জাতীয় আন্দোলন : কলিকাতা ১৯৬৫: পৃঃ ৮৩)
নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘স্বপ্নময়ী’ নাটক সম্পর্কে গবেষক ডঃ প্রভাতকুমার গোস্বামীর সত্যভাষণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি লিখেছেন, …..কিন্তু কাহিনী যেভাবে সাজানো হয়েছে তাতে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার অবকাশ ছিল কম। এতে যা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ। অত্যাচারী শুধু রাজশক্তি নয়, গোটা মুসলমান সমাজই। স্বপ্নময়ী বলছেনঃ
……দেবমন্দির সকল
চূর্ণচূর্ণ করিতেছে ম্লেচ্ছ পদাঘাতে,
বেদমন্ত্র ধর্মকর্ম করিতেছে লোপ
গোহত্যা নির্ভয়ে করে রাজপথ মাঝে। (৩/৩)
এই শুভসিংহের উক্তির হুবহু প্রতিধ্বনি। অন্যত্র সুরজমল বলেছেন : “যেখানে মুসলমান থাকে সেখানকার বাতাসও যেন আমার বিষতুল্য বোধ হয়।” (ডঃ প্রভাতকুমার গোস্বামী : দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক বাংলা নাটকঃ ১৩৮৫ সাহিত্য প্রকাশ, কলিকাতা )
এ ধরনের বিরাজমান নিদারুণ এক পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সত্ত্বেও মানব প্রেমিক রবীন্দ্রপ্রতিভার বিচ্ছুরণকে কেউই প্রতিহত করতে পারেনি। উদ্দাম জনরাশির মতো এই প্রতিভা সম্মুখপানে ধাবিত হলো। পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের যেসব ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন সেগুলো হচ্ছে— কবিতা, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প এবং প্রবন্ধ। এসবের মধ্যে তাঁর রচিত কাব্য সম্ভারকে অগাধ সমুদ্র হিসেবে উল্লেখ যথার্থ হবে। গবেষকরা আলোচনার সুবিধার্থে রবীন্দ্র কাব্যকে সূচনা পর্ব, উন্মেষ পর্ব, ঐশ্বর্য পর্ব, অন্তর্বর্তী পর্ব, গীতাঞ্জলী পর্ব, বলাকা পর্ব এবং অন্তপর্ব এই ৭টি অধ্যায়ে চিহ্নিত করেছেন।
এক্ষণে ধাপেধাপে রবীন্দ্রনাথের মনমানসিকতা কিভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ নাগাদ গড়ে উঠেছিলো, তা সঠিকভাবে অনুধাবনের লক্ষ্যে রবীন্দরনাথ ঠাকুরের ‘বিসর্জন’ নাটকটি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা অপরিহার্য বলে মনে হয়। ‘বিসর্জন’ (১৮৯০) নাটকটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘রাজর্ষি’ নামক উপন্যাস-এর প্রথমাংশ নিয়ে পাত্র-পাত্রী কিছু অদলবদল করে রচনা করেছেন। ‘রাজর্ষি’-এর কাহিনী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, “এটি আমার স্বপ্নলব্ধ গল্প। এমন স্বপ্নে পাওয়া গল্প এবং অন্য লেখা আমার আরো আছে।” (রচনাবলী সংস্করণের ভূমিকা এবং ‘জীবন স্মৃতি’)
১৮৯০ সালে রচিত ‘বিসর্জন’ নাটকটি স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের রাজপরিবারের ভ্রাতৃ কলহের উপর ভিত্তি করে রচিত। এই তত্ত্ববাহী নাটকটির কোথাও ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনও হিংসাত্মক প্ররোচনা কিংবা দেশাত্মবোধক কোনও সংলাপ পর্যন্ত নাই। নাটকটির তত্ত্ববাহী বক্তব্য হচ্ছে, প্রেমের পথ ও হিংসার পথ এক নয়। হিংসার পথে দেবতার পূজা হয় না। প্রেমেই কেবলমাত্র তা সম্ভব। কিন্তু ‘বিসর্জন’ নাটকের মূল বক্তব্যকে এড়িয়ে শুধুমাত্র সিংহাসনের দাবীদার দুই বৈমাত্রেয় ভাই-এর কলহের হিসেবে পার্শ্বচরিত্র জয়সিংহ এবং রাজপুরোহিতদের সংলাপের জন্য কোলকাতার তৎকালীন পুলিশ নাটকটি লালবাজার থানায় আটক করে। রাজ পুরোহিত রঘুপতির একটি সংলাপ হচ্ছেঃ
“……কে বলিল হত্যাকাণ্ড মাপ।
এজগৎ মহা হত্যাশালা।”
অবশ্য পরবর্তীকালে বাধ্য হয়ে ‘বিসর্জন’ নাটকটির অংশ বিশেষ (ইংরেজ আমলে পুলিশের দৃষ্টিতে আপত্তিকর) বাদ দিলে মঞ্চস্থ করার অনুমতি দেয়া হয়।
ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এতসব কর্মকাণ্ডের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ বারবার তাঁর মুক্তবুদ্ধি মনমানসিকতার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন। উত্তেজনা ও ভাবপ্রবণতার আবরণে সংকীর্ণতা কিংবা সাম্প্রদায়িকতা তাঁকে পথভ্রষ্ট করতে পারেনি। মানব প্রেম এবং শাশ্বত প্রকৃতির প্রতি তাঁর নিরবিচ্ছিন্ন প্রেমকে তিনি সব কিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিভংগী ছিলো স্বচ্ছ এবং পরিচ্ছন্ন। তাই তিনি মূল শত্রু পরাশক্তি ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি বিপ্লবীর ভূমিকায় অবতীর্ণ না হয়েও তাঁর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব প্রকাশে দ্বিধা বোধ করেন।
১৮৯৯-১৯০২ সালে ইংরেজরা প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়র জাতির স্বাধীনতা হরণ করলে রবীন্দরনাথের কবিতা হচ্ছেঃ
শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে
অস্ত গেল, হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উম্মাদ, রাগিনী
ভয়ংকরী। দয়াহীন সভ্যতানাগিনী
তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমেষে
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে।…..
(নৈবেদ্য ৬৪ এবং ৬৫ নং কবিতা)
এই প্রেক্ষাপটে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দীনবন্ধু মিত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী। আর বাকী প্রায় সবারই বক্তব্য মোটামুটিভাবে একসূত্রে গাঁথা। একটু অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখলেই বোঝা যায় যে, এঁদের কোথাও কোন ছন্দ পতন নেই। পরাশক্তির শাসনকে মেনে নিয়ে কোলকাতা কেন্দ্রিক এক শক্তিশালী বাঙালি বর্ণ হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও মধ্যশ্রেণী গড়ে তোলাই ছিলো এঁদের উদ্দেশ্য। তাই সে আমলের কবি, সাহিত্যিক নাট্যকার, সমাজ সেবক, ধর্মপ্রচারক আর রাজনীতিবিদ সবারই লক্ষ্য ছিল এক ও অভিন্ন।
তাইতো ১৭৫৭ সাল থেকে শুরু করে ১৯০৫ সালের বংগভংগ পর্যন্ত প্রায় দেড়শ’ বছরে ছোটবড় মিলিয়ে প্রায় ৪০টির মত কৃষক বিদ্রোহের কোনটাই এঁদের সমর্থন লাভ করেনি : বরং চরম বিরোধিতা পেয়েছে। এঁরা ছিলেন সব সময়েই সমাজ ও শ্রেণী সচেতন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, বহু ঘাত-প্রতিঘাতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ বাঙালি-গুজরাটি-মারাঠা মিলনের মাঝ দিয়ে যখন এঁরা ছত্রপতি শিবাজীর বীরত্ব গাঁথাকে কেন্দ্ৰ করে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে “হিন্দু রিভাইভালিজম”-এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলো, ঠিক তখনই লর্ড কার্জনের বংগভংগ সিদ্ধান্ত সব কিছুকেই লণ্ডভণ্ড করে দিলো। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ‘হিন্দু রিভাইভালিজম’-এর মূল চালিকা শক্তি কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি বর্ণ হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্তরা নিজেদের অস্তিত্ব এবং প্রভুত্ব রক্ষার তাগিদে পৃষ্ঠপোষক ইংরেজ রাজশক্তির সংগে তাঁদের এতদিনের মিত্রতা বিনষ্ট করে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লো।
সমসাময়িককালের এই চাঞ্চল্যকর প্রেক্ষিতে বংগভংগ বিরোধী আন্দোলনের পুরোধায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগমন এবং কিয়ৎকালের মধ্যে এই আন্দোলনের সংগে রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কচ্ছেদের ইতিহাস বিশেষভাবে লক্ষণীয়।
বংগভংগের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক কারণসমূহ ছাড়াও কোন্ প্রেক্ষাপটে কোলকাতা কেন্দিরক বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী মহল আর বিত্তশালী সম্প্রদায় বংগভংগবিরোধী আন্দোলনে “হিতাহিত জ্ঞানশূন্য” অবস্থায় মেতে উঠেছিলো ইতিপূর্বে তা সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হয়েছে। এক্ষণে রবীন্দ্রনাথ ও বংগভংগবিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা বাঞ্ছনীয় মনে হয়। ১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট কোলকাতার টাউন হলে প্রস্তাবিত বংগভংগের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত বিরাট জনসভায় বৃটিশ পণ্যদ্রব্য বর্জনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সভায় যেসব শ্লোগান উচ্চারিত হয়, সেগুলো হচ্ছে, “সংযুক্ত বাংলা চাই”, “ব্যবচ্ছেদ চাই না” এবং “বন্দেমাতরম” ইত্যাদি। এর মাত্র ১৮ দিন পর ২৫শে আগষ্ট বংগভংগের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আরও একটি জনসভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর লিখিত ‘অবস্থা ও ব্যবস্থা’ প্রবন্ধটি পাঠ করেন। এতে তিনি ‘স্বদেশী’ ও ‘বয়কট’ সংক্রান্ত কয়েকটি বিতর্কমূলক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। স্বাভাবিকভাবেই সে আমলের চরমপন্থী বর্ণহিন্দু নেতৃবৃন্দের নিকট এই আলোচনা খুব একটা মনঃপুত হয়নি।
অতঃপর ২২শে সেপ্টেম্বর কোলকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত জনসভায় ‘মিলন মন্দির’ তৈরীর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯০৫ সালের ৯ই অক্টোবর ছিলো হিন্দুদের ‘বিজয়ী দশমী।’ এই দিন কোলকাতার বাগবাজারে পশুপতি বসু মহাশয়ের বাসভবনে অনুষ্ঠিত সভায় রবীন্দ্রনাথ ‘বিজয়া সম্মেলন’ নামে এক ভাষণদান করেন।
এই ঐতিহাসিক ভাষণের অংশবিশেষ নিম্নরূপ :
“হে বন্ধুগণ, আজ আমাদের বিজয়া সম্মিলনের দিনে হৃদয়কে একবার আমাদের এই বাংলাদেশের সর্বত্র প্রেরণ করো। যে চাষি চাষ করিয়া এতক্ষণে ঘরে ফিরিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো, যে রাখাল ধেনুদলকে গোষ্টগৃহে এতক্ষণে ফিরাইয়া আনিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো, অস্তসূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে মুসলমান নামাজ পড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো।…… একবার করজোড়ে করিয়া নতশিরে বিশ্বভুবনেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো-
বাংলার মাটি বাংলার বায়ু,
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
বাঙালির প্রাণ, বাঙালির ঘরে
এক হউক এক হউক
বাংলার জল, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক হে ভগবান।….
বাঙালির মন, যতো ভাইবোন
এক হউক হে ভগবান।”
(রচনাবলী পৃষ্ঠাঃ ১০৮৫-১০৮৯)
এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, সে আমলে বাঙালি বৰ্ণহিন্দু নেতৃবৃন্দ যখন সম্প্রদায়গত স্বার্থে বংগভংগবিরোধী আন্দোলনে দারুণভাবে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিলো, তখন ঘটনা প্রবাহে আন্দোলনের পুরোভাগে অবস্থান করেও দুরদৃষ্টিসম্পন্ন রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা ও মনমানসিকতা ছিলো বেশ কিছুটা ভিন্নধর্মী। ‘বংগদর্পণ’ পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে এসময় রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলিম মিলনের লক্ষ্যে “রাখী বন্ধন” অনুষ্ঠানের প্রস্তাব উত্থাপন করেন।
ফলে ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর (১৩১২ বংগাব্দের ৩০শে আশ্বিন) আইনগতভাবে বংগভংগের দিনটিতে বংগভংগ বিরোধীরা তাঁদের কর্মসূচীতে “রাখীবন্ধন”-এর অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত করেন। এদিন সমগ্র বাংলায় সভা-সমিতি, ‘হরতাল’ এবং ‘অরন্ধন’ ইত্যাদি কর্মসূচী পালন করা হয়। “অরন্ধন” অর্থাৎ কোন গৃহের রন্ধনশালার চুল্লীতে আগুন না জ্বালানোর প্রস্তাবক ছিলেন প্রখ্যাত প্রবন্ধকার আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, ঐদিন সকালে ‘বন্দেমাতরম’ গান গেয়ে প্রভাত ফেরী ও শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। এই শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণকারীরা গংগায় অবগাহন করে। এরপর বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে “রাখীবন্ধন” অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এসময় অসংখ্য পথচারীর হাতে “রাখী” বেঁধে দেন। বিকেলে রোগজর্জর প্রবীণ ব্রাহ্মণনেতা আনন্দ মোহন বসুর উদ্যোগে কোলকাতার ২৯৪ আপার সার্কুলার রোডে প্রায় ৫০ হাজার লোকের সমাবেশে প্রস্তাবিত মিলন মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। গবেষক হেমেন্দ্রনাথ রচিত ‘ভারতের জাতীয় কংগ্রেস’ (২য় খণ্ড পূঃ ৩৩-৩৫) গ্রন্থ মোতাবেক এই অনুষ্ঠানে আনন্দমোহন বসুর লিখিত ইংরেজী ভাষণটি পাঠ করেন আশুতোষ চৌধুরী (প্রমথ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) এবং বাংলায় অনুবাদ করে পাঠ করেছিলেন রবীন্দরনাথ।
মিলন মন্দিরের অনুষ্ঠানের পর এক বিরাট জনতা নগ্নপদে শোভাযাত্রা সহকারে বংগভংগ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা পশুপতি বসু মহাশয়ের বাগবাজারের বাসভবনে গমন করে। এখানে উল্লেখ্য যে, শোভাযাত্রীরা সেদিন রবীন্দ্রনাথের সদ্যরচিত যে দু’টি গান সমবেত কণ্ঠে গেয়েছিলো, সে দু’টি হচ্ছেঃ
ক. ‘ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে, ততই বাঁধন টুটবে।’
খ. ‘বিধির বিধান কাটবে তুমি এমন শক্তিমান।’
(গীতবিতান ১, পৃঃ ২৬৫-২৬৬)
‘আমার সোনার বাংলা’ গান রবীন্দ্রনাথের অমর সৃষ্টি
কবি রবীন্দ্রনাথ এসময় মাতৃভূমির বন্দনামূলক অনেক ক’টি সংগীত যে রচনা করেছিলেন তাই-ই নয়, তিনি এসব সংগীতের মাধ্যমে গণমানুষের হৃদয়কে জয় করার জন্য সবিশেষ প্রচেষ্টা করেছিলেন। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিলো, এসব সংগীত যেনো অচিরেই একটা সার্বজনীন আবেদন সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। এজন্যই রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িককালে তাঁর রচিত অধিকাংশ সংগীতে অত্যন্ত সার্থকভাবে কীর্তন, বাউল, লালন, রামপ্রসারী ইত্যাদি লোকসংগীতের সুর ব্যবহার করেছিলেন। ঠিক এমনি সময়ে রবীন্দ্রনাথের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি হচ্ছে, “আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।” রবীন্দ্রনাথ সেদিন চিন্তাও করতে পারেননি যে, ইতিহাসের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে মাত্র ৬৬ বছরের ব্যবধানে কোলকাতাসহ পশ্চিম বংগীয় রাঢ় অঞ্চলকে বাদ দিয়ে গাংগেয় বদ্বীপ এলাকার সমন্বয়ে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হবে এবং প্রকৃত বাঙালি জনগোষ্ঠীর আবাসভূমি এই বাংলাদেশ তাঁরই রচিত ‘আমার সোনার বাংলা’ গানকে জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণ করবে। আর এই বাংলাদেশই নতুন উদ্যমে নিরবিচ্ছিন্নভাবে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ইতিহাস এবং বাঙালি সংস্কৃতির চর্চার পাঠস্থানে পরিণত হবে।
তবে তিনি এটুকু অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, সমসাময়িককালে বাংলা ভাষা-ভাষী এলাকায় কোলকাতা কেন্দ্রিক ইংরেজী শিক্ষিত বর্ণহিন্দু বিত্তশালী ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় যেভাবে সংখ্যাগুরু বাঙালি মুসলমানদের অবহেলিত ও হেয় প্রতিপন্ন করে যাচ্ছে তার ফল কোন অবস্থাতেই শুভ হতে পারে না। তিনি নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, বর্ণহিন্দু সমাজ সংগঠনের বৈশিষ্ট্য এবং ঐতিহ্য হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার মৌল উৎস এবং এর ঢক্কা নিনাদ হচ্ছে অনাগত ভবিষ্যতের বিপদ সংকেত। এ জন্যই তিনি দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে লিখলেন :-
“মানুষকে ঘৃণা করা যে দেশের ধর্মের নিয়ম, প্রতিবেশীর হাতে জল খাইলে যাহাদের পরকাল নষ্ট হয়, পরকে অপমান করিয়া যাহাদিগকে জাতিরক্ষা করিতে হইবে, পরের হাতে অপমানিত না হইয়া তাহাদের গতি নাই। তাহারা যাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে সেই ম্লেচ্ছের অবজ্ঞা তাহাদিগকে সহ্য করিতে হইবেই।….. আমরা (বর্ণহিন্দুরা) যে কেবল স্বতন্ত্র তাহা নয়। আমরা বিরুদ্ধ। আমরা বহুশত বৎসর পাশে পাশে থাকিয়া এক খেতের ফল, এক নদীর জল, এক সূর্যের আলোক ভোগ করিয়া আসিয়াছি, আমরা এক ভাষায় কথা কই, আমরা একই সুখ-দুঃখে মানুষ, তবু প্রতিবেশীর সংগে প্রতিবেশীর যে সম্বন্ধ মনুষ্যোচিত যাহা ধর্মবিহিত, তাহা আমাদের মধ্যে হয় নাই। আমাদের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এমন একটি পাপ আমরা পোষণ করিয়াছি যে, একত্রে মিলিয়াও আমরা বিচ্ছেদকে ঠেকাইতে পারি নাই। এ পাপকে ঈশ্বর কোনোমতেই ক্ষমা করতে পারেন না। ….. আমাদের পাপই ইংরেজদের …… প্রধান বল।” (রচনাবলী ১২, পৃঃ ৯০৫-৯১৪)।
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের হুঁশিয়ারিতেও নেতৃবৃন্দের কোনরূপচৈতন্য হলো না বলা যায় বংগভংগ বিরোধী আন্দোলন তার আপন গতিতে ধাবিত হলো। একদিকে নরমপন্থী বর্ণহিন্দু রাজনীতিবিদদের শূন্যগর্ভ বাগ্মিতায় সাময়িক উত্তেজনা আর অন্যদিকে সনাতন হিন্দু ধর্মের আবরণে অর্থাৎ কালী মন্দিরে দীক্ষা ও শপথ গ্রহণ অন্তে ভয়ংকর সন্ত্রাসের সূচনা। আন্দোলনের সর্বস্তরেই মানব-প্রেম আর উদার হৃদয়ের মারাত্মক অভাব রবীন্দ্রনাথের হৃদয়কে ব্যথিত করে তুললো। পরবর্তীকালে তিনি স্বীয় মানসিক অবস্থা সম্পর্কে লিখেছেন :-
“হিন্দু-পল্লীতে বাধার অন্ত নেই। হিন্দুধর্ম হিন্দুসমাজের মূলেই এমন একটা গভীর ব্যাঘাত রয়েছে, যাতে করে সমবেত লোকহিতের চেষ্টা অন্তর থেকে বাধা পেতে থাকে। এই সমস্ত প্রত্যক্ষ দেখে হিন্দুসমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধে ‘আইডিয়ালাইজ’ কোনো আত্মঘাতী শ্রুতিমধুর মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিতে আমার ইচ্ছাই হয় না।” (জীবনী ২ পৃঃ ২২৯)।
তাহলে একথা আজ নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বংগভংগবিরোধী আন্দোলনের সংগঠন পর্বে এবং প্রারমিভক পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকলেও নানা অর্থবহ কারণে অচিরাৎ তাঁর মধ্যে ব্যাপক মানসিক দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। সহকর্মীদের মধ্যে সংকীর্ণ ধর্মীয় মনোভাব, এক শ্রেণীর নেতৃবৃন্দের উত্তেজনাময় শূন্যগর্ভ বক্তৃতা, গ্রাম উন্নয়নের সুষ্ঠু প্রস্তাবনার অভাব, রক্তাক্ত সন্ত্রাসের গুপ্ত পদ্ধতি এবং হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক সমস্যার প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের চিন্তারাজ্যে দারুণ আলোড়নের সৃষ্টি হলো। সামগ্রিকভাবে দেশের গণমানুষের কল্যাণের পরিবর্তে শুধুমাত্র কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি বর্ণহিন্দু বিত্তশালী ও বুদ্ধিজীবীদের স্বার্থে পরিচালিত বংগভংগ বিরোধী আন্দোলনের সংগে সংযুক্ত থাকার বিষয়টাতে তিনি স্বীয় বিবেকের সমর্থন পেলেন না।
তাই ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ১৯০৫ সালে কবি রবীন্দ্রনাথ বংগভংগবিরোধী আন্দোলনের রাজনৈতিক উত্তেজনার সামিল ছিলেন মাত্র মাস তিনেকের জন্য। এরপর তিনি অসংখ্য বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী এবং মানুষকে বিস্মময়বিমূঢ়. করে স্বদেশী আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ান। এসময় দেশে বিরজমান সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা তাঁর মনকে দারুণভাবে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিলো। তিনি কিংকর্তব্যবিমুঢ়. হয়ে পড়লেন। পরবর্তীতে তার এই মানসিক অবস্থা সম্পর্কে কালিদাস নাগকে লিখিত এক পত্রে মন্তব্য করলেন, “হিন্দু ধর্মকে ভারতবাসী প্ৰকাণ্ড একটা বেড়ার মতো করেই গড়ে তুলেছিল। এর প্রকৃতিই হচ্ছে নিষেধ এবং প্রত্যাখ্যান। সকল প্রকার মিলনের পক্ষে এমন সুনিপুণ কৌশলে রচিত বাধা জগতে আর কোথাও সৃষ্টি হয়নি। এই বাধা কেবল হিন্দু-মুসলমানে তা নয়। তোমার আমার মতো মানুষ যারা আচারে স্বাধীনতা রক্ষা করতে চাই, আমারও পৃথক, বাধাগ্রস্ত। সমস্যা তো এই, কিন্তু সমাধান কোথায়?………
ধর্মকে কবরের মতো তৈরী করে তারই মধ্যে সমগ্র জাতিকে ভূতকালের মধ্যে সর্বতোভাবে নিহিত করে রাখলে উন্নতির পথে চলবার উপায় নেই, কারও সংগে কারও মেলবার উপায় নেই। আমাদের মানসপ্রকৃতির মধ্যে যে অবরোধ রয়েছে তাকে ঘোচাতে না পারলে আমরা কোনো রকমের স্বাধীনতাই পাব না। শিক্ষার দ্বারা, সাধনার দ্বারা, সেই মূলের পরিবর্তন ঘটাতে হবে— ডানার চেয়ে খাঁচা বড়ো এই সংস্কারটাকেই বদলে ফেলতে হবে— তার পরে আমাদের কল্যাণ হতে পারবে। হিন্দু-মুসলমানের মিলন যুগপরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে। (রচনাবলী ১৩, পৃঃ ৩৫৭)
বংগভংগ বিরোধী আন্দোলনের সময় এক শ্রেণীর বর্ণহিন্দু নেতৃবৃন্দের উত্তেজনাময় শূন্যগর্ভ বক্তৃতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ছিলো না। তিনি এসবের তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, “দেশে যদি বর্তমানকালে এইরূপ লোকেরই সংখ্যা এবং ইহাদেরই প্রভাব অধিক থাকে তবে আমাদের মতো লোকের কর্তব্য নিভৃতে যথাসাধ্য নিজের কাজে মনোযোগ করা। উন্মাদনায় যোগ দিলে কিয়ৎপরিমাণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেই হয় এবং তাহার পরিণামে অবসাদ ভোগ করিতেই হয়। আমি তাই ঠিক করিয়াছি যে, অগ্নিকাণ্ডের আয়োজনে উন্মত্ত না হইয়া যতদিন আয়ু আছে, আমার এই প্রদীপটিকে জ্বালিয়া পথের ধারে বসিয়া থাকিব। (জীবনী ২, পৃঃ ১৭৫)
এসব কারণের জের হিসেবে এবং প্রচণ্ড মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মাঝ দিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আকস্মিক সিদ্ধান্তে সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ালেন। এসময় তাঁর চিন্তা রাজ্যের প্রতিক্রিয়ার প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে পাই, ‘বিদায়’, ‘প্রতীক্ষা’ এবং ‘সব-পেয়েছির দেশ’ প্রভৃতি কবিতায়। এসব কবিতায় তিনি অক্ষমতার কথা বলে রাজনীতির বিগত দিনের সহযাত্রীদের নিকট ক্ষমা প্রর্থনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বিনীতভাবে স্বীয় বক্তব্য উপস্থাপিত করে বলেছেন যে, তাঁর দৃষ্টিতে বিগত দিনের রাজনৈতিক আদর্শ মিথ্যা এবং মূল্যহীন। ‘বিদায়’ শীর্ষক কবিতায় তিনি লিখলেন :-
“রত্ন খোঁজা, রাজ্য ভাষা গড়া,
মতের লাগি দেশ-বিদেশে লড়া,
আলবালে জলসেচন করা
উচ্চ শাখা স্বর্ণচাপার গাছে।
পারি নে আর চলতে সবার পাছে।”
(রচনাবলী ২, পৃঃ ১৯৫-১৯৬)
এখানে উল্লেখ্য যে, বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে প্রথমে বংগভংগ বিরোধী আন্দোলনের ডামাডোল এবং এরই প্রেক্ষাপটে রক্তাক্ত সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত হলে কবিগুরু রবীন্দনাথ যখন আদর্শগত কারণে এসবের সম্পর্কচ্ছেদ করলেন, তখন কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এবং পত্র-পত্রিকাগুলো তাঁকে “ইংরেজ শাসকের পক্ষভুক্ত” চিহ্নিত করে কিভাবে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছিলো, এক্ষণে সংক্ষিপ্তভাবে হলেও তাঁর কিঞ্চিৎ বর্ণনা বাঞ্ছনীয় মনে হয়। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকার রামেন্দ্রসুন্দুর ত্রিবেদী এ সময় লিখলেন, “দু’বৎসর ধরিয়া মাতামাতির পর কতকটা স্নায়ুবিক অবসাদে, কতকটা ইংরেজের ভ্রুকুটিদর্শনে আমরা এখন ঠান্ডা হইয়া পড়িয়াছি। রবিবাবুও সময় বুঝিয়া আমাদিগকে বলিতেছেন মাতামাতিতে বিশেষ কিছু হইবে না, এখন কাজ করো। ……. স্বদেশী আগুন যখন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তখন রবীন্দ্রনাথের লেখনী তাহাতে বাতাস দিতে ত্রুটি করে নাই। বেশ মনে ৩০শে আশ্বিনের পূর্ব হইতে হপ্তায় তাঁহার এক একটা নূতন গান বা কবিতা বাহির হইত, আর আমাদের স্নায়ুতন্ত্র কাঁপিয়া আর নাচিয়া উঠিত। নিস্ফল ও অনাবশ্যক আন্দোলনে তিনি কখনোই উপদেশ দেন নাই, কিন্তু সে সময়টায় যে উত্তেজনা ও উন্মাদনা ঘটিয়াছিল, তাহার জন্য রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব নিতান্ত অল্প ছিল না। উত্তেজনার বশে আমরা দুই বৎসর ধরিয়া ইংরেজে’র অনুগ্র লইব না, ইংরেজের শাসনতন্ত্র অচল করিয়া দিব বলিয়া লাফালাফি করিয়া আসিতেছি। এবং ইংরেজ রাজা যখন সেই লাফালাফিতে ধৈর্যভ্রষ্ট হইয়া লগুড় তুলিয়া আমাদের গলা চাপিয়া ধরিয়াছেন, তখন আমাদের সেই অস্বাভাবিক আস্ফালনের নিস্ফলতা দর্শনে ব্যথিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন— ওপথে চলিলে হইবে না— মাতামাতি লাফালাফির কর্ম নহে, নীরবে ধীরভাবে কাজ করিতে হইবে।” (প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৪, রচনাবলী ১০, পৃঃ ৬৬৪-৬৬৫)
এসময় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর রচিত ‘স্বদেশী ধুয়া’, ‘জাতীয় একতা’ এবং ‘স্বদেশ প্রেমের ব্যাধি’ ইত্যাদি প্রবন্ধে রবীন্দ্র দৃষ্টিভংগীর সমালোচনা করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। ‘স্বদেশ প্রেমের ব্যাধি’ নিবন্ধে শ্রী শাস্তরী এ মর্মে মন্তব্য করলেন যে, স্বদেশ প্রেম আদর্শ হিসেবে অতীতকে গোরবান্বিত করে, উন্নতিবিধানের কথা বলে না, এবং যা ভবিষ্যৎ প্রগতির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তা প্রেম নয়, ব্যাধি।’ সমালোচক প্রমথনাথ রায় চৌধুরী রবীন্দ্রনাথ-এর ভূমিকার প্রতি কটাক্ষ করে মন্তব্য করলেন, “কাজ নিশ্চয়ই, কিন্তু কথাও বা নয় কেন? অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আমরা বন্ধ করব কেন? স্বীকার করি, অনেক কথা বাজে খরচ করা হয়েছে, কিন্তু তার সবই কি সম্পূর্ণ বিফল হয়েছে?” (সুমিত সরকারকৃত দি স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেংগল, পৃঃ ৫৮)
গোত্রান্তরিত রবীন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ জবাবদান
কিন্তু রবীন্দ্র রচনাবলী সঠিকভাবে পাঠ করলে দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাথও যথাসময়ে এসব সমালোচনার বলিষ্ঠ জবাব দিয়েছেন। সে আমলে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা যথার্থ পর্যালোচনা করলে একথা নিশ্চিতভাবে অনুধাবন করা যায় যে, বংগভংগ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্বদানের মাত্র মাস তিনেক সময়ের মধ্যে তাঁর পক্ষে আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ানো খুবই অর্থবহ ছিলো। স্বদেশী আন্দোলন থেকে শুধু সরে দাঁড়ানোই নয়— রবীন্দ্রনাথ এরপর প্রায় এক বছরকাল নিশ্চুপ ছিলেন। যখন কবি আবার কর্মক্ষেত্রে ফিরে এলেন, তখন তাঁর ভিন্ন রূপ— ভিন্ন পথ এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে, তিনি এসময় সম্পূর্ণ ভিন্নদর্শে পথযাত্রী হলেন। রবীন্দ্রনাথের মনন জগতে উত্তরণ হলো। গবেষক ডঃ অরবিন্দ পোদ্দারের মতে, “আসলে এমনিভাবেই তাঁর মধ্যে দিয়ে কালের আন্তর গরজ অভিব্যক্তি লাভ করে; বলা যায়, এর বিবর্তন ঘটে প্রায় দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের পারস্পর্যের পথে। …….. বৈপ্লবিক মনোভংগী ও কর্মপন্থা তিনি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ঘৃণা করেছেন, স্বদেশী আন্দোলন থেকে রবীন্দ্রনাথের সরে দাঁড়ানো নিছক সরে দাঁড়ানো নয়, এ যেন তাঁর গোত্রান্তর। নিঃসন্দেহ যে, এই আন্দোলন যে জটিল আবর্তের সৃষ্টি করে তা থেকে কিছু কিছু সমস্যা উদ্ভূত হয় যা চিন্তাশীল মানুষকে স্বভাবতঃই উদ্বিগ্ন করে; এর প্রধান হলো হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সমস্যা।…. এ যেন তাঁর মানসপ্রকৃতির অন্য এক অভ্যুদয়। এই নতুন অভ্যুদয়ের আলোকে তিনি ফেলে আসা স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের কঠোর নিস্পৃহ মূল্যায়নে প্রবৃত্ত হন।”
এসব ঘটনার প্রায় দশ বছর পরে ১৯১৬ সাল নাগাদ, অর্থাৎ নোবেল পুরস্কার লাভেরও বছর তিনেক অতিবাহিত হলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করলেন তাঁর অনন্য সাধারণ উপন্যাস ‘ঘরে-বাইবে’। অতীতে যারা ‘নীতিভ্রষ্ট’, ‘কাপুরুষ’ এবং ‘পলায়নী’ ‘মনোবৃত্তি’ হিসেবে তাঁকে চিহ্নিত করেছিলেন, এই উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি সুতীক্ষ্ণ ভাষায় জবাব দান করলেন। ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসে নিখিলেশ-এর মুখ-নিসৃত সংলাপে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য স্থান পেলো। এর একটি বক্তব্য হলো, “আজ সমস্ত দেশের ভৈরবীচক্রে মদের পাত্র নিয়ে আমি যে বসে যাইনি, এতে সকলের অপ্রিয় হয়েছি। দেশের লোক ভাবছে, আমি খেতাব চাই কিম্বা পুলিশকে ভয় করি। পুলিশ ভাবছে, ভিতরে আমার কুমতলব আছে বলেই বাইরে আমি এমন ভালোমানুষ। তবু আমি এই অবিশ্বাস ও অপমানের পথেই চলেছি। কেননা, আমি এই বলি, দেশকে সাদাভাবে সত্যভাবে দেশ বলেই জেনে, মানুষকে মানুষ বলেই শ্রদ্ধা করে, যারা তার সেবা করতে উৎসাহ পায় না— চীৎকার করে মা বলে, দেবী বলে মন্ত্র পড়ে যাদের কেবল সম্মোহনের দরকার হয়— তাদের সেই ভালোবাসা দেশের প্রতি তেমন নয় যেমন নেশার প্রতি। সত্যের উপরে কোনো একটা মোহকে প্রবল করে রাখবার চেষ্টা, এ আমাদের মজ্জাগত দাসত্বের লক্ষণ।”
এরই পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ বংগভংগ বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী বর্ণহিন্দু রাজনীতিবিদদের চরিত্র কংকন করেছেন ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসের সন্দ্বীপ-এর মধ্যে। সন্দ্বীপ হচ্ছে নিখিলেশের বন্ধু। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চোখে সন্দ্বীপ হচ্ছে লোভী, বিবেকহীন এবং ইন্দ্রীয়পরায়ণ। বন্ধু নিখিলেশের স্ত্রী বিমলার প্রতি সন্দ্বীপের দৃষ্টি কামাতুর। সন্দ্বীপের সংলাপ হচ্ছে, “আমি তাই অন্যায়ের তপস্বাকেই প্রচার করি। আমি সকলকে বলি, অন্যায়ই মোক্ষ, অন্যায়ই বহ্নিশিখা; সে যখনই দগ্ধ না করে তখনই ছাই হয়ে যায়। যখনই কোনো জাত বা মানুষ অন্যায় করতে অক্ষম হয় তখনই পৃথিবীর ভাংগা কুলোয় তার গতি”।
অবশ্য ১৯০৮ সালে রচিত ‘প্রায়শ্চিত্ত’ নাটকেও রবীন্দ্রনাথের এই গোত্রান্তরিত চিন্তাধারার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘স্বদেশী সমাজ’ বক্তৃতায় এবং ‘সদুপায়’, ‘দেশহিত’, ‘পথ ও পাথেয়’, ‘ব্যাধি ও প্রতিকার’ প্রভৃতি নিবন্ধে একই মনমানসিকতা প্রদর্শনে কুণ্ঠাবোধ করেননি। রবীন্দ্র রচনাবলী ১২, পৃষ্ঠা নং- ৯১৮-৯২০-তে সংকলিত ‘দেশহিত’ প্রবন্ধে তিনি স্বদেশী রাজনীতিবিদদের উদ্দেশে লিখেছেন, “কিন্তু যেখানে আমাদের স্বদেশের লোক আমাদের যজ্ঞের পবিত্র হুতাশনে পাপ পদার্থ নিক্ষেপ করিয়া আমাদের হোমকে নষ্ট করিতেছে, তাহাদিগকে আমরা কেন সমস্ত মনের সহিত ভর্ৎসনা করিবার, তিরষ্কৃত করিবার শক্তি অনুভব করিতেছি না। তাহারাই কি আমাদের সকলের চেয়ে ভয়ংকর শত্রু নহে, অধর্ম যেখানে যে নামে যে বেশেই প্রবেশলাভ করিয়াছে সেইখানেই ভয়ংকর সর্বনাশ সাধন করিয়াছে, আমরা শনির সংগে কলির সংগে আপাততঃ সন্ধি করিয়া মহৎ কার্য উদ্ধার করিব এমন ভ্রম আমাদের দেশে কোথাও যদি প্রবেশ করে তবে আমাদের দেশের মহাকবিদের শিক্ষা মিথ্যা ও আমাদের দেশের মহাঋষিদের সাধনা ব্যর্থ হইবে।”
রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে তার বক্তব্য আরও সুস্পষ্ট ভাষায় উপস্থাপিত করলেন। “স্বরাজ তো আকাশ-কুসুম নয়, একটা কার্যপরম্পরার মধ্য দিয়া তো তাহাকে লাভ করিতে হইবে নূতন বা পুরাতন যে দলই হউন তাঁহাদের সেই কাজের তালিকা কোথায়? তাঁহাদের প্লান কি? তাঁহাদের আয়োজন কি? কর্মশূন্য উত্তেজনায় এবং অক্ষম আস্ফালনে একদিন একান্ত ক্লান্তি ও অবসাদ আনিবেই— ইহা মনুষ্য স্বভাবের ধর্ম— কেবল মদ যোগাইয়া আমাদিগকে সেই বিপদে যেন লইয়া যাওয়া না হয়।”….
সমসাময়িককালে রবীন্দ্র মনমানসিকতার উত্তরণ সম্পর্কে পশ্চিম বাংলার বিশিষ্ট গবেষক ডক্টর অরবিন্দ পোদ্দার-এর মূল্যায়ন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি লিখেছেন, “সেই প্রতিক্রিয়া ব্যাপকতায় এত উপপ্লাবী যে, ১৯০৬ সনের মাঝামাঝি থেকে ১৯০৭ সনের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় এক বছর তাঁর রাজনৈতিক কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ ছিল। আর সেই নীরবতা যখন তিনি ভংগ করলেন, দেখা গেল তাঁর কণ্ঠে অন্য সুর আরেক ভাষা। এ যেন অন্য এক রবীন্দ্রনাথ, স্বদেশী যুগের ঐশ্বর্যশীল অভিব্যক্তিতে প্রাণবন্ত রবীন্দ্রনাথ থেকে গুণগতভাবে স্বতন্ত্র। দেশের সার্বিক রাজনৈতিক পরিবেশ, বিশেষতঃ নিছক বাগ্মিতায় অভ্যস্ত নেতৃবৃন্দের মনোভংগীর সমালোচনায় তিনি অধিকতর নিমর্ম ও বলিষ্ঠ এবং বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ও কর্মপন্থার বিরুদ্ধে তাঁর আক্রমণ অপ্রত্যাশিত রকমের প্রচণ্ড; হিংস্র। অপর পক্ষে, তিনি স্বয়ং এক কল্পনাতীত রাজনৈতিক বন্দরের অভিমুখে সমুদ্রাভিসারে উদ্যোগী”। (রবীন্দ্রনাথ/ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব— পৃঃ ১৪৬, ‘উচ্চারণ কলিকাতা)
এ সময় রবীন্দ্রনাথের মানসিক দ্বন্দ্ব এবং চিন্তাধারার বিশেষণ করে পশ্চিম বাংলার বিশিষ্ট গবষেক ও শিক্ষাবিদ ডঃ অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় যে সত্যভাষণ করেছেন তা’ এক কথায় অপরূপ এবং বস্তুনিষ্ঠ। তিনি লিখেছেন, “বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বংগভংগ আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন স্বয়ং কবিগুরু। সে আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল, বাঙালি ও ভারতীয় জীবনধারার সামগ্রিকভাবে উন্নয়ন, শুধু বিদেশী শাসকশক্তির বিরুদ্ধে নিষ্ফল উত্তেজনা সৃষ্টি নয়। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে জীবনের সর্বাংগীন বিকাশ এবং স্বাদেশিক আন্দোলন হঠাৎ রাজনৈতিক দলাদলি, উগ্র জাতীয়তাবাদ, সন্ত্রাসবাদী হিংসা, স্বদেশীয়ানার ছদ্মবেশে ব্যক্তিগত লোভলালসা এবং হিন্দুয়ানির ছদ্মবেশে সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি উগ্র হয়ে জাতির শুভবুদ্ধিকে গ্রাস করে নিল। রবীন্দ্রনাথ মনের আকাশকে কখনোও খন্ড খর্ব করে দেখতে চাননি, স্বদেশ প্রেমের স্থলে রক্তশোষী উগ্র জাতীয়তাবাদ সমর্থন করেননি, শাসকের বিরুদ্ধে গুপ্ত অভিযানের রক্তাক্ত পরিণাম কোন দিন মেনে নিতে পারেননি।” (বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, ৪র্থ সং, পৃঃ ৬২৯)
ডঃ বন্দোপাধ্যায় এ সম্পর্কে আরও লিখেছেন, “কিন্তু তিনি (রবীন্দ্রনাথ) বেশীদিন এইভাবে আত্মরসে নিমগ্ন থাকতে পারলেন না। বংগভংগ আন্দোলন উপলক্ষে যুব শক্তি যখন সন্ত্রাসবাদের গোপন গুহায় বিস্ফোরক সঞ্চিত করছিল, রবীন্দ্রনাথ সেই রাজনৈতিক দলাদলি ও রক্তাক্ত বিদ্বেষের মধ্যে আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। সন্ত্রাসবাদের চাপা গর্জনকে উপেক্ষা করে খেয়াতরী নিয়ে অকূলে ভাসলেন। ক্লান্ত কবি বলে উঠলেন : “বিদায় দেহ ক্ষম আমার ভাই, কাজের পথে আমি তো আর নাই।”
এবার কবি দলাদলি, দলভাংগা প্রভৃতি বিষয় থেকে সম্পূর্ণরূপে বিদায় নিলেন। কারণ তখন তিনি ক্লান্তশ্রান্ত চিত্তে ওপারের দিকে চেয়ে “দুঃখযামিনীর বুকচেরা ধন” প্রত্যক্ষ করলেন- এবার ‘চিত্রা’ ‘কল্পনার জগৎ ছেড়ে নতুন জগতের দিকে তিনি খেয়া নৌকা ভাসালেন— এ হল ‘গীতাঞ্জলি’, ‘গীতালি’ ও ‘গীতিমাল্যে’র যুগ। একদিকে রূপজগৎ আর একদিকে অরূপজগৎ— এই দুয়ের মাঝখানে ‘খেয়ার’ জগৎ। খেয়া নৌকা যেমন এ ঘাট থেকে অপর ঘাটে পাড়ি দেয়, তেমনি কবি প্রেম-সৌন্দর্যের জগৎ ছেড়ে ভক্তি ও আধ্যাত্ম সাধনার জ্যোতির্ময়লোকে যাত্রা করলেন। (তদেব, পৃঃ ৫৯৭)
বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক সময়ে বাংলা সাহিত্যের বিরাজমান অবস্থা এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতি কোলকাতা কেন্দ্রিক প্রভাবশালী বর্ণ হিন্দু লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে আরও কিছুটা আলোকপাত করা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা ‘সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত’ গ্রন্থের ২৩তম পরিচ্ছদে এ ব্যাপারে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের ক্ষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি লিখেছেন, “বিশ শতকের গোড়ার দিকে বঙ্কিমপ্রভাবের রেশ মিলিয়ে যায়নি, রবীন্দ্র প্রতিভার যথার্থ স্বরূপ সম্বন্ধেও অনেকের সংশয় ঘোচেনি। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বিপিনচন্দ্র পাল— এ’রা রবীন্দ্র সাহিত্য ও আদর্শ সম্বেন্ধে এই সময় থেকেই প্রতিকূল স্রোতে সমালোচনার তরণী ভাসিয়েছিলেন, কেউ কেউ দুর্নীতির অভিযোগ এনে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সাহিত্য সাধনাকে অপদস্থ করতে চেয়েছিলেন। এ যুগের উগ্র রাজনৈতিক আন্দোলনের একচক্ষু নীতি কবিগুরু সমর্থন করেননি। যিনি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অন্যতম উৎসাহী নেতা ছিলেন, তিনি এর মধ্যে রক্তাক্ত সন্ত্রাসবাদের গূঢ় চারী গতায়াত দেখে এর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য আশ্রম স্থাপন করলেন এবং মানুষ তৈরীর কাজে আত্মসমর্পণ করলেন। তাঁর এই রাজনৈতিক অনীহাকে কেউ কেউ ভীরুতা অপবাদে নিন্দা করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে সমাজে ব্রাহ্ম মতাদর্শ স্বাভাবিক কারণে হীনবল হয়ে পড়লে এবং সংস্কারকামী হিন্দু সমাজ পুনরুত্থিত হলে তাঁকে ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত মনে করে কেউ কেউ তাঁর সর্ববিধ কর্মের প্রতিও উদাসীন হয়ে পড়লেন। দ্বিজন্দ্রলাল রায় রবীন্দ্রনাথের ‘গীতাঞ্জলি’ পর্বের গানগুলির বিরুদ্ধে অস্পষ্টতার এবং ‘চিত্রাঙ্গদা’র বিরুদ্ধে দুর্নীতিপূর্ণ অশ্লীলতার অভিযোগ আনলেন, তাঁকে নিন্দা করার জন্য ‘আনন্দবিদায়’ নামে বিদ্রুপপূর্ণ রঙ্গনাট্য লিখলেন। অবশ্য তার জন্য তিনি সকলের কাছে নিন্দিতও হয়েছিলেন।
“ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পুরাণাচারী হিন্দুধর্মের যে পুনরুত্থান ঘটল, তারই মুখপাত্র হিসেবে যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর ‘বঙ্গবাসী’ (১৮৮১), কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের সম্পাদনায় প্রকাশিত ‘হিতবাদী” (১৮৯১), সুরেশচন্দ্র সমাজপতির ‘সাহিত্য’ (১৮৯০) প্রভৃতি পত্রে হিন্দুধর্ম ও সমাজবিষয়ক কিছু কিছু রক্ষণশীল মত প্রচারিত হতে শুরু করল। অপরদিকে ‘সঞ্জীবনী’ পত্রিকা আবার বিপরীত দৃষ্টিকোণ থেকে যা কিছু হিন্দুর পৌরাণিক সংস্কার, তাকেই যেন বিদ্ধ করতে লাগল। ১৮৯৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধান হলে নব্য-হিন্দুধর্মের প্রচারক তাঁর শিষ্য সম্প্রদায়ের কেউ কেউ উল্লিখিত হিন্দুসমাজের মুখপত্রস্বরূপ পত্রিকাগুলিতে যোগদান করলেন, যাঁদের অনেকেই রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমর্থক ছিলেন না। বিশেষতঃ রবীন্দ্র রচনা এমন একটা সূক্ষ্ণ মানসিক অনুশীলন ও স্থিতধী চেতনারসের বস্তু যে, দ্বৈরথ সমরে অভিলাষী সূক্ষ্ণবোধহীন ব্যক্তির পক্ষে তার গহনে প্রবেশ করা এক প্রকার দুঃসাধ্য। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রসাহিত্য জনপ্রি হয়েছিল। অবশ্য তাঁর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ এসে পৌছলে রবীন্দ্রবিরোধী বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের বিষোদগার যে একেবারে বন্ধ হয়ে গেল তা নয়। একটু পরবর্তীকালে যখন রবীন্দ্র প্রতিভা মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো খ্যাতির তুঙ্গ শিখরে উঠেছে, তখনও কোন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি নিন্দার তূণ থেকে দুটি-চারটি শায়ক নিক্ষেপ করতে লাগলেন। অবশ্য এবার বিরোধ ব্যক্তিগত নয়, সাহিত্যাদর্শ নিয়েই তাঁর সঙ্গে নবীন ও প্রাচীনের দল বিবাদ-বিতর্কে প্রবৃত্ত হলেন। অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শরৎচন্দ্র এবং নবীনতর সাহিত্যিকেরা রবীন্দ্রসাহিত্য যথেষ্ট বাস্তব নয় এবং তাতে যুগযন্ত্রণা ফোটেনি, এই ধরনের অর্ধসামাজিক প্রশ্ন তুলেছিলেন। এদের কারও কারও সঙ্গে তিনি বিতর্কে অবতীর্ণ হতেও বাধ্য হন।”
রবীন্দ্র-সংকলন থেকে ‘শিবাজী উৎসব’ কবিতা বাদ হলো
এজন্যই আমরা রবীন্দ্র প্রতিভার মূল্যায়নকালে দেখতে পাই, যে রবীন্দ্রনাথ ১৯০৪ সালে সখারাম দেউস্কর কৃত ‘শিবাজীর দীক্ষা’ গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে যেয়ে শিবাজীর বন্দনা করে ‘শিবাজী উৎসব কবিতা রচনা করেছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীতে তাঁর চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন হওয়ায় কোন কোন সংকলন থেকে এই কবিতাটি বাদ পর্যন্ত দিয়েছিলেন। ‘শিবাজী উৎসব’ কবিতার কয়েকটি পংক্তি নিম্নরূপ :
‘মারাঠার সাথে আজি হে বাঙ্গালি
এক কন্ঠে বলো জয়তু শিবাজী
মারাঠার সাথে আজি হে বাঙ্গালি
এক সংগে চলো মহোৎসবে সাজি।’
কোন কোন সংকলন থেকে আলোচ্য কবিতাটি বাদ দেয়া ছাড়াও পরবর্তীতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এসব ব্যাপারে অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ভাষায় স্বীয় বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। তিনি লিখেছেন, “….তার মধ্যে আবার আজকাল এক উৎপাত জুটেছে, আমার কর্তাদের মাথায় ঢুকেছে ইতিহাস রক্ষা, — কোথা থেকে সব কবর খুঁড়ে এনে হাজির করে বলে আমার রচনা, সে দেখলে লজ্জায় মরে যাই। বলতে ইচ্ছে করে সে তোমার লেখা, কিন্তু তা হবার নয়- ছাপার অক্ষরে একবার কালি পড়লে সে কলঙ্গ আর ঘুচবে না, ইতিহাস রক্ষা! আরে কাব্যের আবার ইতিহাসের দরকার কি? তার মূল্য তার আপনার মধ্যেই আছে, ফুলের মূল্য বুঝতে গেলে কি তার শিকড় উৎপাটন করতে হবে? সৃষ্টিকর্তা আপনিও তো তাঁর নিজের রচনা সংশোধন করে চলেছেন। নির্মম হাতে মুছে ফেললেন কত অসমাপ্ত সৃষ্টি। কত পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে আজকের মানুষ তৈরী হয়েছে,— সে সব চাপা পড়ে গেল, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।” [মৈত্রেয়ী দেবী কৃত ‘মংপুতে রবীন্দ্রনাথ’ : ১০ম মুদ্রণঃ ১৯৮৫, কলিকাতা]
‘আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে গো ফুল ফুটবে’ -রবীন্দ্রনাথ
তা’হলে একথা যথার্থভাবে বলা যায় যে, বংগভংগ বিরোধী আন্দোলনের উত্তপ্ত পরিবেশে কবি রবীন্দ্রনাথের গোত্রান্তর হলো। তাঁর অন্তর্যামী সুদূর দিগন্তের সীমারেখা ছেড়ে অসীমে পানে ধাবিত হলো। দীনতা, হীনমন্যতা এবং সংকীর্ণতা সবকিছুকেই তিনি আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করলেন। সাম্প্রদায়িক সমস্যার জটিলতা তাঁর মানস জগতে যে উথাল-পাতালের সৃষ্টি করেছিলো, রবীন্দ্রনাথ সেই সংঘাতের পীড়ন থেকে মুক্তিলাভে সক্ষম হলেন। তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন মানবিক মূল্যবোধের মর্যাদাকে— তিনি মানব গোষ্ঠীর অবিভাজ্য চেতনার মাঝে স্বীয় আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। রবীন্দ্রপ্রতিভা নতুন সূর্যালোকে সমুজ্জ্বল হলো। তিনি মানবপ্রেম এবং বিশ্বপ্রেমের সুগভীর সলিলে অবগাহন করে নবজন্ম লাভ করলেন অচিরকালের মধ্যে তাঁর লেখনী দিয়ে সৃষ্টি হলো তিন তিনটি অমর কবিতাঃ
ক) হে মোর চিত্ত, পূণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে—
খ) যেথায় থাকে সবার অধম দীন হতে দীন
গ) হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুহৃদ শ্রী কালিদাস নাগ মহাশয়কে প্রেরিত পত্রে স্বীয় চিন্তাধারার মর্মবাণী সুস্পষ্ট ভাষায় লিখলেন, “…শুভ চেষ্টা দ্বারা দেশকে জয় করিয়া লও— যাহারা তোমাকে সন্দেহ করে তাহাদের সন্দেহকে জয় করো, যাহারা তোমার প্রতি বিদ্বেষ করে তাহাদের বিদ্বেষকে পরাস্ত করো, রুদ্ধদ্বারে আঘাত করো, বারম্বার আঘাত করো— কোনো নৈরাশ্য, কোনো আত্মাভিমানের ক্ষুণ্ণতায় ফিরিয়া যাইয়ো না, মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদয়কে চিরদিন কখনোই প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না।” (রচনাবলী ১২ পৃঃ, ১০০৩)
সত্যিকারভাবে বলতে গেলে, গীতাঞ্জলি পর্বে এসে রবীন্দ্রপ্রতিভা পূর্ণতা লাভ করলো। মানবপ্রেম, বিশ্বপ্রেম, বৈষ্ণববাদ আর সুফী মতবাদের উদারতার সজীব স্পর্শে এই প্রতিভা সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করলো। গবেষক ডঃ অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়ের মতে “…… আবার এই পর্বটির বৈশিষ্ট্য বিচার করে একে রবীন্দ্র কবি জীবনের আধ্যাত্মপর্বও বলতে পারা যায়। কারণ এই তিনখানি (গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালি) গীতিসংগ্রহের মূলকথা কবির সংগে তার ঈশ্বরচেতনার অংগাংগিসম্বন্ধ। এর আগে ‘খেয়া’ কাব্যে দেখা গেছে, কবি বস্তুলোকের ঘাট ছেড়ে অন্তর্লোকের সুদৃঢ়. যাত্রী হতে চেয়েছেন….. গীতাঞ্জলিতে সেই অন্তর্লোকের রহস্য ধরা দিয়েছে। কবি এই গীতি সংগ্রহে অন্ত দেবতাকে প্রিয়রূপে সখারূপে, প্রাণেশরূপে— মানবসম্পর্কের বিভিন্ন রূপ ও রসের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করলেন।… তীব্র বিরহের আর্তি ও মিলনের পিপাসা আধ্যাত্ম রেণুরঞ্জিত হয়ে এই গীতিনিবেদনকে সত্যকারের কাব্যরূপ দান করেছে। ‘চিত্রা’ থেকে ‘কল্পনা”, ‘খেয়া’ পর্যন্ত জীবনদেবতা, মানসসুন্দরী অন্তর্যামী প্রভৃতির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের যে কবিমানস বৃহত্তর উপলব্ধির দিকে অগ্রবর্তী হচ্ছিল, ‘গীতাঞ্জলি’তে তারই স্বাভাবিক বিকাশ ও পরিণাম লক্ষ্য করা যাবে। যাঁরা কাব্য থেকে ব্যক্তিচেতনার গভীর আধ্যাত্ম উপলব্ধি বাদ দিতে চান, তাঁরা পৃথিবীর অনেক শ্রেষ্ঠ কাব্য থেকে বঞ্চিত হবেন— রবীন্দ্রনাথকেও যথার্থ ধরতে পারবেন না।…… ‘গীতালি’-তে আধ্যাত্ম চেতনার আর এক ধরনের বৈচিত্র্য দেখা গেল। এটি মূলতঃ গীতিসংগ্রহ— তত্ত্ব নয়, আধ্যাত্ম সাধনাও নয়। কবির প্রাণেশ দেখা দিলেন প্রেমিকের বেশে— এবং উভয়ের মধ্যে লীলারসের সম্পর্ক ফুটে উঠলো! তাই কবি সার্থক আনন্দের সুরে বলে উঠলেন, “আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে গো ফুল ফুটবে।” (বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্তঃ ৪র্থ সংস্করণঃ পূঃ ৫৯৮-৫৯৯)
প্রাসংগিক বিধায় এখানে একটা কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, রবীন্দ্রদর্শন এবং সুফী মতবাদের মধ্যে অপূর্ব সাদৃশ্য বিদ্যমান। সুফী মতবাদ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যাদান করলে, বিষয়টা বোধগম্য হবে। সুফীরা সব সময়ের পবিত্র কোরানের সমর্থনকে সম্বল করে জীবন ও ধর্মকে সমন্বিত করার প্রচেষ্টা করেছেন। ভোগে পরিমিতবাদের সূত্র ধরে বৈরাগ্যবাদও প্রশ্রয় পেয়েছে সুফীতত্ত্বে। সুফী ধর্ম হচ্ছে প্রেমের ধর্ম। এ প্রেম হচ্ছে আল্লাহর প্রতি প্রেম। সৃষ্টি প্রেমেই স্রষ্টা প্রেমের বিকাশ। মরণ নদীর এপারে-ওপারে পরিব্যপ্ত জীবনের নির্দ্বন্দ্ব উপলব্ধিতেই সুফী সাধনার সিদ্ধি। তাই সুফী সাধকদের বক্তব্য হচ্ছে, ‘আত্ম-বিস্মৃত হয়ে সবাইকে প্রেম, ভালবাসা ও প্রীতি দান করো এবং অপরের কল্যাণ কর্মে আত্ম-নিয়োগ করো।’
এই প্রেক্ষাপটে বিচার করলে আমরা দেখতে পাই যে, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝ দিয়ে গোত্রান্তরিত রবীন্দ্রনাথ পরিণত হলেন মানব পূজারি হিসেবে। রবীন্দ্র-অন্তরের সবটাই জুড়ে উদ্ভাসিত হলো শাশ্বত প্রকৃতির প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম। এ প্রেম বৈদান্তবাদের নিরাকার ঈশ্বরের প্রেম— এ প্রেম বৈষ্ণব ভাবালুলতার প্রেম এবং সবশেষে এ প্রেম হচ্ছে সুফী দর্শনের ‘আশিক-মাশুক’-এর প্রেম। বিশেষ কোন ধর্মীয় অন্ধতা কিংবা রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের কুটিলতা ও হানাহানি এবং হিংসা ও বিদ্বেষ প্রচারণা এ সবকিছুই রবীন্দ্রপ্রতিভাকে আচ্ছন্ন করা দূরের কথা, আর স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারলো না। নূতন উপলব্ধিতে উদ্ভাসিত রবীন্দ্রনাথ তার বিখ্যাত ‘সোনার তরী’ কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় অপরূপ অভিব্যক্তি প্রকাশ করলেন। তিনি লিখলেন, “কতবার সমস্ত বৎসর ধরে পদ্মার আতিথ্য নিয়েছি, বৈশাখের খররৌদ্রতাপে, শ্রাবণের মুষলধারা বর্ষণে। পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যামশ্রী, এপারে ছিল বালুচরের পাণ্ডুবর্ণ জনহীনতা, মাঝখানে পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দ্যুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানা বর্ণের আলোছায়ার তুলি। এইখানে নির্জন-সজনের নিত্য সংগম চলেছিল আমার জীবনে। অহরহ সুখ-দুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবযাত্রার বিচিত্র কলরব এসে পৌঁছাচ্ছিল আমার হৃদয়ে। মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল।…. আমার বুদ্ধি এবং কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল এই সময়কার প্রবর্তনা— বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবলোকের মধ্যে নিত্যসচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা।”
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সব রকমের সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে এক মহান ব্যক্তিত্ব আর বিশাল প্রতিভায় পরিণত হলেন। সার্বজনীন স্বীকৃতির জের হিসেবে তিনি পরিচিত হলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ হিসেবে। তিনি ‘ঝড়ের খেয়া’ কবিতায় মানব-প্রেমিকদের প্রতি উদাত্ত কণ্ঠে আহবান জানালেন,
“যাত্রা কর যাত্রা কর,
যাত্রী দল এসেছে আদেশ”