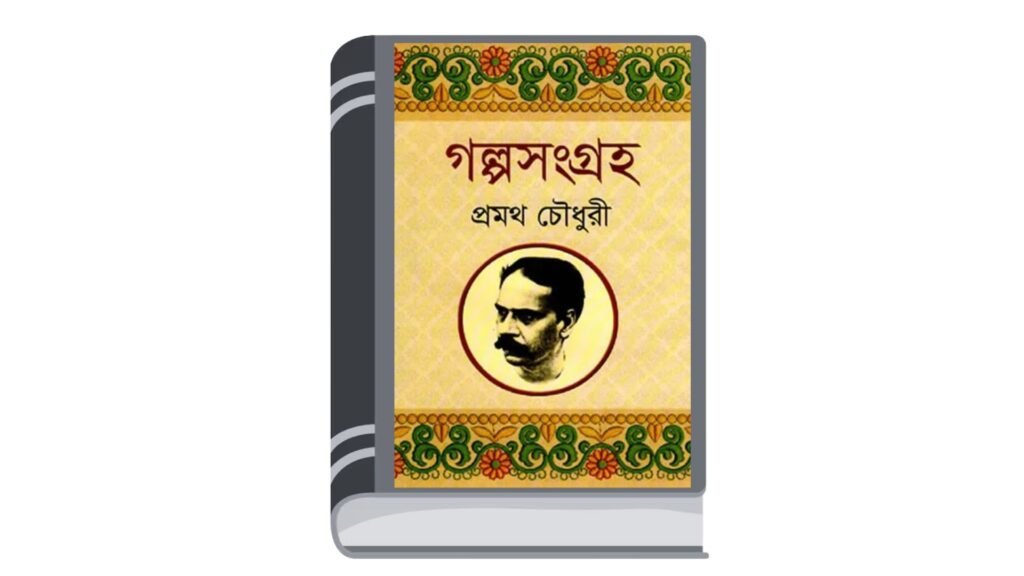বড়োবাবুর বড়োদিন
বড়োদিনের ছুটিতে বড়োবাবু যে কেন থিয়েটার দেখতে যান, যে কাজ তিনি ইতিপূর্বে এবং অতঃপর কখনো করেন নি, সেই এক একদিনের জন্য সে কাজ তিনি যে কেন করেন, তার ভিতর অবশ্য একটু রহস্য আছে। তিনি যে আমোদপ্রিয় নন, এ সত্য এতই স্পষ্ট যে, তাঁর শত্রুরাও তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করত। তিনি বাঁধাবাঁধি নিয়মের অতিশয় ভক্ত ছিলেন, এবং নিজের জীবনকে বাঁধা নিয়মের সম্পূর্ণ অধীন করে নিয়ে এসেছিলেন। পনেরো বৎসরের মধ্যে তিনি একদিনও আপিস কামাই করেন নি, একদিনও ছুটি নেন নি, এবং প্রতিদিন দশটা-পাঁচটা ঘাড় গুঁজে একমনে খাতা লিখে এসেছেন। আপিসের বড়োসাহেব Mr. Schleiermacher বলতেন, ““ফবানী’ মানুষ নয়—কলের মানুষ; ও দেহে বাঙালি হলেও মনে খাঁটি জর্মান।” বলা বাহুল্য যে, ‘ফবানী’ হচ্ছে ভবানীরই জর্মান সংস্করণ। এই গুণেই, এই যন্ত্রের মতো নিয়মে চলার দরুনই তিনি অল্পবয়সে আপিসের বড়োবাবু হয়ে ওঠেন। সে সময়ে তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশের বেশি দিন ছিল না, যদিচ দেখতে মনে হত যে তিনি পঞ্চাশ পেরিয়েছেন। চোখের এরকম ভুল হবার কারণ এই যে, অপর্যাপ্ত এবং অতিপ্রবৃদ্ধ দাড়িগোঁফে তাঁর মুখে বয়সের অঙ্ক সব চাপা পড়ে গিয়েছিল। বড়োবাবু যে সকলপ্রকার শখ-সাধ আমোদ-আহ্লাদের প্রতি শুধু বীতরাগ নয়, বীতশ্রদ্ধও ছিলেন, তার কারণ আমোদ জিনিসটে কোনোরূপ নিয়মের ভিতর পড়ে না। বরং, ও বস্তুর ধর্মই হচ্ছে সকলপ্রকারের নিয়ম ভঙ্গ করা। ‘রুটিন’ করে আমোদ করা যে কাজ করারই শামিল, এ কথা সকলেই মানতে বাধ্য। উৎসব ব্যাপারটি অবশ্য নিত্যকর্মের মধ্যে নয়, এবং যে কর্ম নিত্যকর্ম নয় এবং হতে পারে না, তাকে বড়োবাবু ভালোবাসতেন না—ভয় করতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, সুচারুরূপে জীবনযাত্রানির্বাহ করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে জীবনটাকে দৈনন্দিন করে তোলা; অর্থাৎ সেই জীবন—যার দিনগুলো কলে তৈরি জিনিসের মতো—একটি ঠিক আর একটির মতো।
বৈচিত্র্য না থাকলেও, বড়োবাবুর জীবন যে নিরানন্দ ছিল, তা নয়।। তাঁর গৃহের কৌটায় এমন একটি অমূল্য রত্ন ছিল, যার উপর তাঁর হৃদয় মন দিবারাত্র পড়ে থাকত। তাঁর স্ত্রী ছিল পরমাসুন্দরী। বাপ-মা তার নাম রেখেছিলেন পটেশ্বরী। এ নামের সার্থকতা সম্বন্ধে তার পিতৃকূলের, তার মাতৃকূলের কেউ কখনো সন্দেহ প্রকাশ করেন নি; তাঁরা সকলেই একবাক্যে বলতেন, এ হেন রূপ পটের ছবিতেই দেখা যায়, রক্তমাংসের শরীরে দেখা যায় না। এমন-কি, চাকর-দাসীরাও পটেশ্বরীকে আরমানি বিবির সঙ্গে তুলনা করত। বড়োবাবুর তাদৃশ সৌন্দর্যবোধ না থাকলেও, তাঁর স্ত্রী যে সুন্দরী-শুধু সুন্দরী নয়, অসাধারণ সুন্দর-এ বোধ তাঁর যথেষ্ট ছিল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি অবশ্য তাঁর স্ত্রীর রূপবর্ণনা করতে পারতেন না, কেননা বড়োবাবু আর যাই হন—কবিও নন, চিত্রকরও নন। তা ছাড়া বড়োবাবু তাঁর স্ত্রীকে কখনো ভালো করে খুঁটিয়ে দেখেন নি। একটি প্রাকৃত কবি বলেছেন যে, তাঁর প্রিয়ার সমগ্ররূপ কেউ কখনো দেখতে পায় নি; কেননা যার চোখ তার যে অঙ্গে প্রথম পড়েছে, সেখান থেকে তার চোখ আর উঠতে পারে নি। সম্ভবত ঐ কারণে বড়োবাবুর মুগ্ধনেত্র পটেশ্বরীর পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত কখনো আয়ত্ত করতে পারে নি। বড়োবাবু জানতেন যে, তাঁর স্ত্রীর গায়ের রঙ কাঁচা সোনার মতো আর তার চোখদুটি সাত-রাজার-ধন কালো মানিকের মতো। এই রূপের অলৌকিক আলোতেই তাঁর সমস্ত নয়ন-মন পূর্ণ করে রেখেছিল। বড়োবাবুর বিশ্বাস ছিল যে, পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলেই তিনি এহেন স্ত্রীরত্ন লাভ করেছেন। এই শাপভ্রষ্ট দেবকন্যা যে পথ ভুলে তাঁর হাতে এসে পড়েছে এবং তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি হয়েছে, এ মনে করে তাঁর আনন্দের আর অবধি ছিল না।
কিন্তু মানুষের যা অত্যন্ত সুখের কারণ, প্রায়ই তাই তার নিতান্ত অসুখের কারণ হয়ে ওঠে। এ স্ত্রী নিয়ে বড়োবাবুর মনে সুখ থাকলেও সোয়াস্তি ছিল না। দরিদ্রের ঘরে কোহিনুর থাকলে তার রাত্তিরে ঘুম হওয়া অসম্ভব। বড়োবাবুর অবস্থাও ঠিক তাই হয়েছিল। এ রত্ন হারাবার ভয় মুহূর্তের জন্যও তাঁর মনকে ছেড়ে যেত না, তাই তিনি সকালসন্ধ্যা কিসে তা রক্ষা করা যায় সেই ভাবনা সেই চিন্তাতেই মগ্ন থাকতেন। আপিসের কাজে তন্ময় থাকাতে, কেবলমাত্র দশটা-পাঁচটা তিনি এই দুর্ভাবনা থেকে অব্যাহতি লাভ করতেন। বড়োবাবুর যদি আপিস না থাকত তা হলে বোধ হয় তিনি ভেবে ভেবে পাগল হয়ে যেতেন।
বড়োবাবুর মনে তাঁর স্ত্রীর সম্বন্ধে নানারূপ সন্দেহের উদয় হত। অথচ সে সন্দেহের কোনো স্পষ্ট কারণ ছিল না। কিন্তু তার থেকে তিনি কোনোরূপ সান্ত্বনা পেতেন না।—কেননা অস্পষ্ট ভয় অস্পষ্ট ভাবনাই আমাদের মনকে সব চাইতে বেশি পেয়ে বসে এবং বেশি চেপে ধরে। তাঁর স্ত্রীকে সন্দেহ করবার কোনোরূপ বৈধ কারণ না থাকলেও বড়োবাবুর মনে তার সপক্ষে অনেকগুলি ছোটোখাটো কারণ ছিল। প্রথমত, সাধারণত স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁর অবিশ্বাস ছিল। ‘বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ স্ত্রী রাজকুলেষু চ’, এ বাক্যের প্রথম অংশ তিনি বেদবাক্য স্বরূপে মানতেন। তার পর তাঁর ধারণা ছিল যে, রূপ আর চরিত্র প্রায় একাধারে পাওয়া যায় না। তাঁর শ্বশুরপরিবারের অন্তত পুরুষদের চরিত্র বিষয়ে তেমন সুনাম ছিল না। পাটের কারবারে হঠাৎ অগাধ পয়সা করায় সে পরিবারের মাথা অনেকটা বিগড়ে গিয়েছিল; ফলে, তাঁর শ্বশুরবাড়ির হালচাল অসম্ভব রকম বেড়ে গিয়েছিল। তাঁর শ্যালক তিনটি যে আমোদ-আহ্লাদ নিয়েই দিন কাটাতেন এ কথা তো শহরসুদ্ধ লোক জানত, এবং এদের ভাইবোনের ভিতর যে পরস্পরের অত্যন্ত মিল ছিল, সে সত্য বড়োবাবুর নিকট অবিদিত ছিল না। ভাইদের সঙ্গে দেখা হলে পটেশ্বরীর মুখ হাসিতে ভরে উঠত, তাদের সঙ্গে তার কথা আর ফুরত না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে অনর্গল বকে যেত, আর হেসে কুটিকুটি হত। এ-সব সময়ে বড়োবাবু অবশ্য উপস্থিত থাকতেন না, তাই এদের কি যে কথা হত তা তিনি জানতেন না। কিন্তু তিনি ধরে রেখেছিলেন যে, তখন যা বলা-কওয়া হত সে-সব নেহাত বাজে কথা। ভাইদের সঙ্গে এই হাসি-তামাসা, তিনি পটেশ্বরীর চরিত্রের আমোদপ্রিয়তার লক্ষণ বলেই মনে করতেন। এ অবশ্য তাঁর মোটেই ভালো লাগত না। বড়োবাবুর স্বভাবটি যেমন চাপা, পটেশ্বরীর স্বভাব ছিল তেমনি খোলা। তার চালচলন কথাবার্তার ভিতর প্রাণের যে সহজ সরল স্ফূর্তি ছিল, বড়োবাবু তাকে চঞ্চলতা বলতেন, এবং এই চঞ্চলতাকে তিনি বিশেষ ভয় করতেন। তার পর পটেশ্বরীর কোনো সন্তানাদি হয় নি, সুতরাং তার যৌবনের কোনো ক্ষয় হয় নি। যদিচ তখন তার বয়স চব্বিশ বৎসর, তবুও দেখতে তাকে ষোলোর বেশি দেখাত না, এবং তার স্বভাব ও মনোভাবও ঐ ষোলো বৎসরের অনুরূপই ছিল। বড়োবাবুর পক্ষে বিশেষ কষ্টের বিষয় এই ছিল যে, এই-সব ভয়-ভাবনা তাঁকে নিজের মনেই চেপে রাখতে হত। পটেশ্বররি কোনো কাজে বাধা দেওয়া কিংবা তাকে কোনো কথা বলা, বড়োবাবুর সাহসে কখনো কুলোয় নি। এমন- কি, বাঙালি ঘরের মেয়ের পক্ষে, বিশেষত ভদ্রমহিলার পক্ষে শিশ্ দেওয়াটা যে দেখতেও ভালো দেখায় না, শুনতেও ভালো শোনায় না—এই সহজ কথাটাও বড়োবাবু তাঁর স্ত্রীকে কখনো মুখ ফুটে বলতে পারেন নি। তার প্রথম কারণ, পটেশ্বরী বড়োমানুষের মেয়ে। শুধু তাই নয়, একমাত্র কন্যা। বাপ-মা-ভাইদের আদর পেয়ে পেয়ে সে অত্যন্ত অভিমানী হয়ে উঠেছিল, একটি রূঢ় কথাও তার গায়ে সইত না, অনাদরের ঈষৎ স্পর্শে তার চোখ জলে ভরে আসত। আর পটেশ্বরীর চোখের জল দেখবার শক্তি আর যারই থাক্ বড়োবাবুর দেহে ছিল না। তা ছাড়া দেবতার গায়ে হস্তক্ষেপ করতে মানুষমাত্রেরই সংকোচ হয়, ভয় হয়; এবং, তাঁর শ্যালকদের বিশ্বাস অন্যরূপ হলেও, তিনি মনুষ্যত্ববর্জিত ছিলেন না। সে যাই হোক, বড়োবাবুর মনে শান্তি ছিল না বলে যে সুখ ছিল না, এ কথা সত্য নয়। বিপদের ভয় না থাকলে মানুষে সম্পদের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। এই-সব ভয়-ভাবনাই বড়োবাবুর স্বভাবত-ঝিমন্ত মনকে সজাগ সচেতন ও সতর্ক করে রেখেছিল। তা পটেশ্বরী সম্বন্ধে তাঁর ভয় যে অলীক এবং তাঁর সন্দেহ যে অকারণ, এ জ্ঞান অন্তত দিনে একবার করেও তাঁর মনে উদয় হত এবং তখন তাঁর মন কোজাগর পূর্ণিমার রাতের মতো প্রসন্ন ও প্রফুল্ল হয়ে উঠত।
বড়োবাবুর মনে শুধু দুটি ভাব প্রবল হয়ে উঠেছিল, স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ, আর ব্রাহ্মসমাজের প্রতি রাগ। ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অবশ্য তাঁর কোনোরূপ বিদ্বেষ ছিল না, কেননা ধর্ম নিয়ে কখনো মিছে মাথা বকান নি। দেবতা এক কি বহু, ঈশ্বর আছেন কি নেই, যদি থাকেন তা হলে তিনি সাকার কি নিরাকার, ব্রহ্ম সগুণ কি নিৰ্গুণ, দেহাতিরিক্ত আত্মা নামক কোনো পদার্থ আছে কি না, থাকলেও তার স্বরূপ কি—এ- সকল সমস্যা তাঁর মনকে কখনো ব্যতিব্যস্ত করে নি, তাঁর নিদ্রার এক রাত্তিরের জন্য ও ব্যাঘাত ঘটায় নি। তিনি জানতেন যে, বিশ্বের হিসাবের খতিয়ান করবার জন্য তিনি জন্মগ্রহণ করেন নি। তবে এর থেকে অনুমান করা অসংগত হবে যে, তিনি নাস্তিক ছিলেন। আমাদের অধিকাংশ লোকের ভূতপ্রেত সম্বন্ধে যে মনোভাব, ঠাকুরদেবতা সম্বন্ধে বড়োবাবুর ঠিক সেইরূপ মনোভাব ছিল—অর্থাৎ তিনি তাদের অস্তিত্বে সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করলেও পুরো ভয় করতেন। আপিসের হয়ে মিথ্যা সাক্ষী দিতে হলে তিনি কালীঘাটে আগে পুজো দিয়ে পরে আদালতে আসতেন—এই উদ্দেশ্যে যে, মা-কালী তাঁকে জেরার হাত থেকে রক্ষা করবেন।
ব্রাহ্মসমাজের ধর্মমত নয়, সামাজিক মতামতের বিরুদ্ধেই তাঁর সমস্ত অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে উঠত। স্ত্রীশিক্ষা স্ত্রীস্বাধীনতা যৌবন-বিবাহ বিধবা-বিবাহ—এ-সকল কথা শুনে তিনি কানে হাত দিতেন। এ-সব মত যারা প্রচার করে তারা যে সমাজের ঘোর শত্রু, সে বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। তাঁর নিজের পক্ষে কি ভালোমন্দ, তারই হিসেব থেকেই তিনি সমাজের পক্ষে কি ভালোমন্দ তাই স্থির করতেন। স্ত্রীস্বাধীনতা?—তাঁর স্ত্রীকে স্বাধীনতা দিলে কি প্রলয় কাণ্ড হবে, সে কথা মনে করতেও তাঁর আতঙ্ক উপস্থিত হত। যিনি নিজের স্ত্রীরত্বকে সামলে রাখবার জন্য ছাদের উপরে ছ হাত উঁচু দরমার বেড়ার ঘের দিয়েছিলেন, যাতে করে তাঁর বাড়ির ভিতর পাড়াপড়শীর নজর না পড়ে—তাঁর কাছে অবশ্য স্ত্রীকে স্বাধীনতা দেওয়া আর ঘরভাঙা—দুই-ই এক কথা। তার পর স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধেও তাঁর ঘোরতর আপত্তি ছিল। স্ত্রীজাতির শরীরের অপেক্ষা মনকে স্বাধীনতা দেওয়া যে কম বিপজ্জনক, এ ভুল ধারণা তাঁর ছিল না। তিনি এই সার বুঝেছিলেন যে, স্ত্রীলোককে লেখাপড়া শেখানোর অর্থ হচ্ছে, বাইরের লোকের এবং বাজে লোকের মনের সঙ্গে তার মনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় করিয়ে দেওয়া। পটেশ্বরী যে সামান্য লেখাপড়া জানত তার কুফল তো তিনি নিত্যই চোখে দেখতে পেতেন। তিনি তাকে যত ভালো ভালো বই কিনে দিতেন—যাতে নানারূপ সদুপদেশ আছে—পটেশ্বরী তার দুই-এক পাতা পড়ে ফেলে দিত; আর সে বাপের বাড়ি থেকে যে-সব বাজে গল্পের বই নিয়ে আসত, দিনমান বসে বসে তাই গিলত। সে-সব কেতাবে কি লেখা আছে তা না জানলেও বড়োবাবু এটা নিশ্চিত জানতেন যে, তাতে যা আছে তা কোনো বইয়ে থাকা উচিত নয়। স্ত্রীলোকের অল্প লেখাপড়ার ভোগ যদি মানুষকে এইরকম ভুগতে হয় তা হলে তাদের বেশি লেখাপড়ার ফলে যে সর্বনাশ হবে, তাতে আর সন্দেহ কি। তার পর যৌবন-বিবাহের প্রচলনের সঙ্গে যে স্বেচ্ছাবিবাহের প্রবর্তন হওয়া অবশ্যম্ভাবী, এ জ্ঞান বড়োবাবুর ছিল। আমাদের সমাজে যদি স্বেচ্ছাবিবাহের প্রথা প্রচলিত থাকত তা হলে বড়োবাবুর দশা কি হত! পটেশ্বরী যে স্বয়ম্বর-সভায় তাঁর গলায় মালা দিতেন না, এ বিষয়ে বড়োবাবু নিঃসন্দেহ ছিলেন। বড়োবাবুর যে রূপ নেই, সে জ্ঞান তাঁর ছিল— কেননা তাঁর সর্বাঙ্গ সেই অভাবের কথা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করত; এবং পটেশ্বরী যে মনুষ্যত্বের মর্যাদা বোঝে না, এ সত্যের পরিচয় তিনি বিবাহাবধি পেয়ে এসেছেন। পটেশ্বরী যে মানুষের চাইতে কুকুর বিড়াল, লাল মাছ, সাদা ইঁদুর, ছাই রঙের কাকাতুয়া, নীল রঙের পায়রা বেশি ভালোবাসত, তার প্রমাণ তো তাঁর গৃহাভ্যন্তরেই ছিল। বাপের পয়সায় তাঁর স্ত্রী তাঁর অন্দরমহলটি একটি ছোটোখাটো চিড়িয়াখানায় পরিণত করেছিল। তার পর বিধবাবিবাহের কথা মনে করতে বড়োবাবুর সর্বাঙ্গ শিউরে উঠত। তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন যে, তিনি স্বর্গারোহণ করলে পটেশ্বরী যদি পত্যন্তর গ্রহণ করে, আর সে সংবাদ যদি স্বর্গে পৌঁছয়, তা হলে সেই মুহূর্তে স্বর্গ নরক হয়ে উঠবে
২
বড়োবাবুর মনের এই দুটি প্রধান প্রবৃত্তি, এই অনুরাগ আর এই বিরাগ, একজোট হয়ে তাঁকে বড়োদিনে থিয়েটারে নিয়ে যায়; নচেৎ শখ করে তিনি অর্থ এবং সময়ের ওরূপ অপব্যয় কখনো করতেন না।
বড়োদিনের ছুটিতে পটেশ্বরী তার বাপের বাড়ি গিয়েছিল। আপিসের কাজ নেই, ঘরে স্ত্রী নেই—অর্থাৎ বড়োবাবুর জীবনের যে দুটি প্রধান অবলম্বন, দুই একসঙ্গে হাতছাড়া হয়ে যাওয়াতে তাঁর কাছে পৃথিবী খালি হয়ে গিয়েছিল। স্ত্রী ঘরে থাকলেও ছুটির দিনে বড়োবাবু অবশ্য বাড়ির ভিতর বসে থাকতেন না। তবে এক ঘরে ফুল থাকলে তার পাশের ঘরটিকে তার সৌরভে যেমন পূর্ণ করে রাখে, তেমনি পটেশ্বরী অন্তঃপুরে থাকলেও অদৃশ্য ফুলের গন্ধের মতো তার অদৃশ্য দেহের রূপে বড়োবাবুর গৃহের ভিতর-বার পূর্ণ করে রাখত। প্রতিমা অন্তর্হিত হলে মন্দিরের যে অবস্থা হয়, পটেশ্বরীর অভাবে তাঁর গৃহের অবস্থাও তদ্রূপ হয়েছিল।
বড়োবাবু এই শূন্য মন্দিরে কি করে দিন কাটাবেন তা আর ভেবে পেতেন না। প্রথমত, তাঁর কোনো বন্ধুবান্ধব ছিল না, তিনি কারো সঙ্গে মেলামেশা করতে ভালোবাসতেন না। গল্প করা কিংবা তাস-পাশা খেলা, এ-সব তাঁর ধাতে ছিল না। তার পর তাঁর বাড়িতে কোনো ভদ্রলোক আসা তিনি নিতান্ত অপছন্দ করতেন। তাঁর স্ত্রীর স্বভাবে কৌতূহল জিনিসটে কিঞ্চিৎ বেশিমাত্রায় ছিল; তার স্বামীর কাছে কোনো লোক এলে পটেশ্বরী খড়খড়ের ভিতর দিয়ে উঁকিঝুঁকি না মেরে থাকতে পারত না।
তার পর সময় কাটাবার একটি প্রকৃষ্ট উপায়—বই পড়া—তাঁর কোনোকালেই অভ্যাস ছিল না। তাঁর বাড়িতেও এমন কেউ ছিল না যার সঙ্গে তিনি বাক্যালাপ করতে পারতেন। তাঁর পরিবারের মধ্যে ছিল, তাঁর স্ত্রী আর তিনি। তিনি গাঁ-সম্পর্কের যে মাসিটিকে পটেশ্বরীর প্রহরীস্বরূপে বাড়িতে এনে রেখেছিলেন, তার সঙ্গে কথা কইতে বড়োবাবু ভয় পেতেন। কেননা ঐ ধার-করা মাসিমাটি তাঁর সাক্ষাৎ পেলেই দুঃখের কান্না কাঁদতে বসতেন, এবং সর্বশেষে টাকা চাইতেন। বড়োবাবু টাকা কাউকেও দিতে ভালোবাসতেন না, আর উক্ত মাসিমাটিকে তো নয়ই; কারণ তিনি জানতেন যে, সে টাকা মাসির গুণধর ছেলেটির মদের খরচে লাগবে। এই-সব কারণে বড়োবাবু নিরুপায় হয়ে দুটি গোটা দিন খবরের কাগজ পড়ে কাটিয়েছিলেন। ওরই মধ্যে একখানিতে একটি বিজ্ঞাপন তাঁর চোখে পড়ল। তাতে তিনি দেখলেন যে, সাবিত্রী থিয়েটারে খৃস্টমাস রজনীতে ‘সংস্কারের কেলেঙ্কার’ নামক প্রহসনের অভিনয় হবে। বলা বাহুল্য, উক্ত প্রহসনের নাম শুনেই সেটির প্রতি তাঁর মন অনুকূল হয়ে উঠল; তার পর তিনি সেই বিজ্ঞাপন হতে এই জ্ঞানসঞ্চয় করলেন যে, উক্ত প্রহসনে সংস্কারকদের উপর বেশ এক হাত নেওয়া হবে। এই বিজ্ঞাপনের প্রলোভনে তাঁর মন ‘সংস্কারের কেলেঙ্কার’এর অভিনয় দেখবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হয়ে উঠল। কিন্তু থিয়েটারে যাওয়া সম্বন্ধে তিনি সহসা মনস্থির করে উঠতে পারলেন না।
তার প্রধান কারণ, তিনি ইতিপূর্বে কখনো থিয়েটারে যান নি; শুধু তাই নয়, তাঁর স্ত্রীর সুমুখে তিনি বহুবার থিয়েটারের বহু নিন্দা করেছেন। থিয়েটারের বিরুদ্ধে তাঁর আক্রোশের কারণ এই ছিল যে, সেখানে ভদ্রঘরের মেয়েরাও যাতায়াত করে। তাঁর মতে অন্তঃপুরবাসিনীদের থিয়েটারে যেতে দেওয়াও যা, আর পত্র-আবডাল দিয়ে স্ত্রী- স্বাধীনতা দেওয়াও তাই। ওর চাইতে মেয়েদের গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে দেওয়া শতগুণে শ্রেয়। আর তিনি যে সময়ে-অসময়ে তাঁর স্ত্রীর কাছে এ বিষয়ে তাঁর কড়াকড়া মতামত সব প্রকাশ করতেন, তার কারণ তিনি শুনেছিলেন যে, থিয়েটার দেখা তাঁর শ্যালাজগণের নিত্যকর্মের মধ্যে হয়ে উঠেছিল। পাছে তাঁর স্ত্রী, তার বৌদিদিদের কুদৃষ্টান্ত অনুসরণ করে, এই ভয়ে তিনি পটেশ্বরীকে শুনিয়ে শুনিয়ে থিয়েটারের বিরুদ্ধে যত কটু কথা প্রয়োগ করতেন। তাঁর মনোগত অভিপ্রায় ছিল, শ্বশুরকুলের বৌকে মেরে ঝিকে শেখানো। এর ফলে পটেশ্বরীর মনে থিয়েটার সম্বন্ধে এমনি একটি বিশ্রী ধারণা জন্মেছিল যে, তার বৌদিদিদের হাজার পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও সে কখনো কোনো থিয়েটারের চৌকাঠ ডিঙয় নি। অন্তত সে তো তার স্বামীকে তাই বুঝিয়েছিল। বড়োবাবু তাঁর স্ত্রী এ কথা বিশ্বাস করতেন; কেননা তা না করলে তিনি জানতেন যে তাঁর মুখের ভাত গলা দিয়ে নামবে না, রাত্তিরে চোখের পাতা পড়বে না, আপিসের খাতায় ঠিক নামাতে ভুল হবে—এক কথায় তাঁর বেঁচে আর কোনো সুখ থাকবে না। এর পর তিনি নিজে যদি সেই পাপ থিয়েটার দেখতে যান, তা হলে তাঁর স্ত্রী কি আর তাঁকে ভক্তি করবে? বলা বাহুল্য, তাঁর স্ত্রীর স্বামীভক্তির উপরে তিনি তাঁর জীবনের সকল আশা, সকল ভরসা প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছিলেন।
এক দিকে স্বচক্ষে সংস্কারকদের লাঞ্ছনা দেখবার অদম্য কৌতূহল, অপর দিকে স্ত্রীর ভক্তি হারাবার ভয়—এই দুটি মনোভাবের মধ্যে তিনি এতদূর দোলাচলচিত্তবৃত্তি হয়ে পড়েছিলেন যে, সমস্ত দিনের মধ্যে তাঁর আর মনস্থির করা হল না। এ ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি উভয়েরই বল সমান ছিল বলে এর একটি অপরটিকে পরাস্ত করতে পারছিল না।
অতঃপর সূর্য যখন অস্ত গেল তখন ‘সংস্কারের কেলেঙ্কার’এর অভিনয় দেখাটা যে তাঁর পক্ষে একান্ত কর্তব্য, এই ধারণাটি হঠাৎ তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়ে গেল। একা বাড়িতে দিনটা বড়োবাবু কোনো প্রকারে কাটালেও ও অবস্থায় সন্ধেটা কাটানো তাঁর পক্ষে বড়োই কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। সেই গোধূলিলগ্নে পটেশ্বরী সম্বন্ধে যতরকম দুশ্চিন্তা সংশয় ভয় ইত্যাদি চাকচিকেবাদুড়ের মতো এসে তাঁর সমস্ত মনটাকে অধিকার করে বসত। তিনি দুদিন এ উপদ্রব সহ্য করেছিলেন, তৃতীয় দিন সহ্য করবার মতো ধৈর্য ও বীর্য বড়োবাবুর দেহে থাকলেও, মনে ছিল না। তিনি স্থির করলেন থিয়েটারে যাবেন, এবং সে কথা পটেশ্বরীর কাছে চেপে যাবেন। তিনি না বললে পটেশ্বরী কি করে জানবে যে তিনি থিয়েটারে গিয়েছিলেন, সে তো আর ও-সব জায়গায় যায় না। এক ধরা পড়বার ভয় ছিল তাঁর শ্যালাজদের কাছে। যদি তারও সে রাত্তিরে ঐ একই থিয়েটারে যায়, এবং সেখানে বড়োবাবুকে দেখতে পায়, তা হলে সে খবর নিশ্চয়ই পটেশ্বরীর কানে পৌঁছবে। যদি তা হয়, তা হলে তিনি অম্লানবদনে সে কথা অস্বীকার করবেন, এইরূপ মনস্থ করলেন; চিকের আড়াল থেকে দেখলে যে লোক চিনতে ভুল হওয়া সম্ভব— এ সত্য তাঁর স্ত্রীও অস্বীকার করতে পারবেন না।
৩
সে রাত্তিরে বড়োবাবু সকাল সকাল খেয়ে দেয়ে—অর্থাৎ এক-রকম না খেয়েই—গায়ে আল্স্টার চড়িয়ে, গলায় কম্ফর্টার জড়িয়ে, মাথা মুখে শাল ঢাকা দিয়ে, সাবিত্রী থিয়েটারের অভিমুখে পদব্রজে রওনা হলেন। পাছে পাড়ার লোক তাঁকে দেখতে পায়, পাছে তাঁর নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের সুনাম একদিনে নষ্ট হয়, এই ভয়ে তিনি নীলনিচোলাবৃত অভিসারিকার মতো ভীতচকিত চিত্তে, অতি সাবধানে, অতি সন্তর্পণে পথ চলতে লাগলেন।
এখানে বলে রাখা আবশ্যক যে তাঁর আস্টারের বর্ণ ছিল ঘোর-নীল, আর নিচোল- পদার্থটি শাড়ি নয়—ওভারকোট। অনাবশ্যক রকম শীতবস্ত্রের ভার বহন করাটা অবশ্য তাঁর পক্ষে মোটেই আরামজনক হয় নি; বিশেষত কমফর্টার নামক গলকম্বলটি তাঁর গলদেশের ভার যে পরিমাণে বৃদ্ধি করেছিল, তার শোভা সে পরিমাণে বৃদ্ধি করে নি। পাঁচ হাত লম্বা উক্ত পশমের গলাবন্ধটি কণ্ঠে ধারণ করা তাঁর পক্ষে একান্ত কষ্টকর হলেও প্রাণ ধরে তিনি সেটি ত্যাগ করতে পারতেন না; তার কারণ পটেশ্বরী সেটি নিজ হাতে বুনে দিয়েছিল। বড়োবাবুর বিশ্বাস ছিল, পাঁচরঙা উলে-বোনা ঐ বস্তুটির তুল্য সুন্দর বস্তু পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। কারুকার্যের ঐ হচ্ছে চরম ফল। সৌন্দর্যে, আকাশের ইন্দ্রধনুর সঙ্গে শুধু তার তুলনা হতে পারত। স্ত্রীহস্ত-রচিত এই গলবস্ত্রটি ধারণ করে তাঁর দেহের যতই অসোয়স্তি হোক, তাঁর মনের সুখের আর সীমা ছিল না। তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করছিলেন যে, পটেশ্বরীর অন্তরের ভালোবাসা যেন সাকার হয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরেছে।
অবশেষে বড়োবাবু থিয়েটারে উপস্থিত হয়ে দেখেন, সে জায়গা প্রায় ভর্তি হয়ে গিয়েছে। এই লোকারণ্যে প্রবেশ করবামাত্র তিনি এতটা ভেবড়ে গেলেন যে নিজের সীটে যাবার পথে এক ব্যক্তির গায়ে ধাক্কা মারলেন, আর-এক ব্যক্তির পা মাড়িয়ে দিলেন। তার জন্য তাঁকে সম্বোধন করে যে-সব কথা বলা হয়েছিল তাকে ঠিক স্বাগত- সম্ভাষণ বলা যায় না।
তখনো drop-scene ওঠে নি, সবে কনসার্ট শুরু হয়েছিল; বেহালাগুলো সব সমস্বরে চিঁ চিঁ করছিল, cello গ্যাঙরাচ্ছিল, bass viola থেকে হুংকার ছাড়ছিল, এবং double bass দ্বিগুণ উৎসাহে হাঁক্কাহোঁক্কা করছিল। তবে ঐ ঐকতান সংগীতের প্রতি বড়ো কেউ যে কান দিচ্ছিলেন না তার প্রমাণ, দর্শকবৃন্দের আলাপের গুঞ্জনে ও হাসির ঝংকারে রঙ্গভূমি একেবারে কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।
তারপর drop-scene যখন পাক খেয়ে খেয়ে শূন্যে উঠে গেল তখন ডজন-দুয়েক অভিনেত্রী লালপরী নীলপরী সবজাপরী জরদাপরী প্রভৃতি রূপে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে খামকা অকারণ নৃত্যগীত শুরু করে দিলে। বড়োবাবুর মনে হল, তাঁর চোখের স্তবকে স্তবকে সব পারিজাত ফুটে উঠল, আর এইসব স্বর্গের ফুল যেন নন্দনবনের মন্দ পবনের স্পর্শে কখনো জড়িয়ে কখনো ছড়িয়ে, ঈষৎ হেলতে-দুলতে লাগল। ক্রমে এই-সকল নর্তকীদের কম্পিত ও আন্দোলিত দেহ ও কণ্ঠ হতে উচ্ছ্বসিত নৃত্য ও গীতের হিল্লোল সমগ্র রঙ্গালয়ের আকাশে বাতাসে সঞ্চারিত হল, সে হিল্লোলের স্পর্শে দর্শকমণ্ডলী শিহরিত পুলকিত হয়ে উঠল। মিনিট-পাঁচেকের জন্য অর্ধচন্দ্রাকারে অবস্থিতি করে এই পরীর দল যখন সবেগে চক্রাকারে ভ্রমণ করতে লাগল, তখন চারি দিক থেকে সকলে মহা উল্লাসে ‘encore’ ‘encore’ বলে চীৎকার করতে লাগল। এত আলো এত রঙ এত সুরের সংস্পর্শে বড়োবাবুর ইন্দ্রিয় প্রথম থেকেই ঈষৎ সচকিত উত্তেজিত হয়েছিল, তার পর সমবেত দর্শকমণ্ডলীর এই তরঙ্গিত আনন্দ তাঁর দেহমনকে একটি সংক্রামক ব্যাধির মতো আক্রমণ করলে। পান করা অভ্যাস না থাকলে একপাত্র মদও যেমন মানুষের মাথায় চড়ে যায় আর তাকে বিহ্বল করে ফেলে, এই নাচ-গান বাজনাও তেমনি বড়োবাবুর মাথায় চড়ে গেল এবং তাঁকে বিহ্বল করে ফেললে। আমোদের নেশায় তাঁর ইন্দ্রিয় একসঙ্গে বিকল হয়ে পড়ল ও চঞ্চল হয়ে উঠল। অতঃপর নেচে নেচে শ্রান্ত ও ঘর্মাক্ত—কলেবর হয়ে নর্তকীর দল যখন নৃত্যে ক্ষান্ত দিলে, তখন একটি স্থূলাঙ্গী বয়স্কা গায়িকা অতি-মিহি অতি-নাকী এবং অতি-টানা সুরে একটি গান গাইতে আরম্ভ করলেন। সে তো গান নয়, ইনিয়ে-বিনিয়ে নাকে-কান্না। বড়োবাবু যে কতদূর কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিলেন, তার প্রমাণ সেই গান যেমনি থামা অমনি তিনি বড়োগলায় ‘encore’ ‘encore’ বলে দু-তিন বার চীৎকার করলেন। তাই শুনে তাঁর এপাশে ওপাশে যে-সব ভদ্রলোক বসে ছিলেন, তাঁরা বড়োবাবুর দিকে কট্ট্ করে চাইতে লাগলেন।
এ গানের যে সুরতালের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না সে জ্ঞান অবশ্য বড়োবাবুর ছিল না; তাই উক্ত ভদ্রলোকদের মধ্যে একটি রসিক ব্যক্তি যখন তাঁকে এই প্রশ্ন করলেন যে, “ঢাকের বাদ্যি থামলেই মিষ্টি লাগে, এ কথা কি মহাশয় কখনো শোনেন নি? আর এটাও কি মালুম হল না যে উনি যে পুরিয়া উদ্গার করলেন, সেটি সরপুরিয়া নয়—ক্যালমেলের পুরিয়া?”—তখন তিনি লজ্জায় অধোবদন ও নিরুত্তর হয়ে রইলেন।
নৃত্যগীত সমাধা হবার পর আবার drop-scene পড়ল, আবার কনসার্ট বেজে উঠল। তাঁতের ছোটো বড়ো মাঝারি বিলিতি যন্ত্রগুলো বাদকদের ছড়ির তাড়নায় গ্যা গোঁ কোঁ প্রভৃতি নানারূপ কাতর ধ্বনি করতে লাগল; ক্লারিওনেট ও করনেট পরস্পরে জ্ঞাতি-শত্রুতার ঝগড়া শুরু করে দিলে এবং অতি কর্কশ আর অতি তীব্র কণ্ঠে, যা মুখে আসে তাই বললে; তার পর ঢোলকের মুখ দিয়ে ঝড় বয়ে গেল; শেষটা করতাল যখন কড় কড় কড়াৎ করে উঠলে তখন কনসার্টের দম ফুরিয়ে গেল। বড়োবাবু ইতিমধ্যে এ-সব গোলমালে কতকটা অভ্যস্ত হয়ে এসেছিলেন, সুতরাং ঐকতান সংগীতের বিলিতি মদ তাঁর অন্তরাত্মাকে এ দফা ততটা ব্যতিব্যস্ত করতে পারলে না।
এর পর নলদময়ন্তী অভিনয় শুরু হল। বড়োবাবু হাঁ করে দেখতে লাগলেন। এ যে অভিনয়, এ জ্ঞান দু মিনিটেই তাঁর লোপ পেয়ে এল, তাঁর মনে হল নলদময়ন্তী প্রভৃতি সত্যসত্যই রক্তমাংসের দেহ ধারণ করে সাবিত্রী থিয়েটারে অবতীর্ণ হয়েছেন। তার পর রঙ্গমঞ্চের উপরে যখন স্বয়ংবর সভার আবির্ভাব হল তখন থিয়েটারের অভ্যন্তরে অকস্মাৎ একটা মহাগোলযোগ উপস্থিত হল। পুরুষদের মাথার উপরে চিকের অপর পারে, রঙ্গালয়ের যে প্রদেশ মেয়েরা অধিকার করে বসেছিলেন, সেই অঞ্চল থেকে একটা ঝড় উঠল। কোনো অজ্ঞাত কারণে সমবেত স্ত্রীমণ্ডলী ঐকতানে কলরব করতে শুরু করলেন। ফলে আকাশে স্ত্রী-কণ্ঠের কন্সার্ট বেজে উঠল, তার ভিতর ক্লারিওনেট করনেট প্রভৃতি সব রকমেরই যন্ত্র ছিল, এবং তাদের পরস্পরের ভিতর কারো সঙ্গে সুরের মিল ছিল না। তার পর সেই কন্সার্ট যখন দুন্ থেকে পরদুনে গিয়ে পৌঁছল, তখন অভিনয় অগত্যা বন্ধ হল। এই কলহ শুনে দময়ন্তীর বড়ো মজা লাগল, তিনি ফিক্ করে হেসে দর্শকমণ্ডলীর দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন, তাঁর সখিরা সব অঞ্চল দিয়ে মুখ ঢাকলেন, আর ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতি অভ্যাগত দেবতাগণ তটস্থ হয়ে রইলেন। অমনি silence! silence! শব্দে চতুর্দিক ধ্বনিত হতে লাগল, তাতে গোলযোগের মাত্রা আরো বেড়ে গেল। অতঃপর দর্শকের মধ্যে অনেকে দাঁড়িয়ে উঠে, আকাশের দিকে মুখ করে, গলবস্ত্রে জোড় করে উক্ত স্ত্রী-সমাজকে সম্বোধন করে ‘মা- লক্ষ্মীরা চুপ করুন’ এই প্রার্থনা করতে লাগলেন; তাতে মা-লক্ষ্মীদের চুপ করা দূরে থাকুক, তাঁদের কোলের ছেলেরা জেগে উঠে ককিয়ে কাঁদতে শুরু করলে। তখন দর্শকদের মধ্যে দু-চার জন ইয়ারগোছের লোক, অতি সাদা বাঙলায় ছেলেদের মুখবন্ধ করবার এমন-একটা সহজ উপায় বাতলে দিলে যা শুনে দময়ন্তী ও তাঁর সখীরা অন্তররুদ্ধ হাসির বেগে ধুঁকতে লাগলেন। বড়োবাবু যদিচ জীবনে কখনো কারো প্রতি কোনোরূপ অভদ্র কথা ব্যবহার করেন নি, তথাচ তিনি ভদ্রমহিলাদের এই অপমানে খুশি হলেন। কেননা, তাঁর মতে যারা থিয়েটারে আসতে পারে, সে-সব স্ত্রীলোকের মানই-বা কি আর অপমানই-বা কি! মিনিট-দশেক পরে, এই গোলযোগ বৈশাখী ঝড়ের মতো যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎ থেমে গেল।
অভিনয় যেখানে থেমে গিয়েছিল, সেইখান থেকে আবার চলতে শুরু করল। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বড়োবাবু সেই অভিনয়ে তন্ময় হয়ে গেলেন। এই অভিনয়-দর্শনে তিনি এতটা মুগ্ধ হয়ে গেলেন যে, তাঁর মনে সাত্ত্বিকভাবের উদয় হল, তাঁর কাছে রঙ্গালয় তীর্থস্থান হয়ে উঠল। তার পর নলদময়ন্তীর বিপদ যখন ঘনিয়ে এল তখন তাঁর মন নায়ক-নায়িকার দুঃখে একেবারে অভিভূত দ্রবীভূত হয়ে পড়ল। নলের দুঃখই অবশ্য তিনি বেশি করে অনুভব করছিলেন, কেননা পুরুষমানুষের মন পুরুষমানুষেই বেশি বুঝতে পারে। নলের প্রতি তাঁর এতটা সহানুভূতির আর-একটি কারণ ছিল। তিনি প্রথম থেকেই লক্ষ্য করেছিলেন যে, তাঁর সঙ্গে ঐ রঙ্গমঞ্চের নলের যথেষ্ট আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে; কিন্তু পটেশ্বরীর সঙ্গে দময়ন্তীর কোনো সাদৃশ্যই ছিল না। নলরাজ বেশ পরিত্যাগ করবার সময় সে সাদৃশ্য এতটা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল যে, মধ্যে মধ্যে বড়োবাবুর মনে ভুল হচ্ছিল যে উক্ত নল তিনি ছাড়া আর কেউ নয়, সুতরাং নল যখন নিদ্রিতা দময়ন্তীর অঞ্চলপাশ মোচন করে, ‘হা হতোহস্মি হা দগ্ধোহস্মি’ বলে রঙ্গমঞ্চ হতে সবেগে নিষ্ক্রমণ করলেন তখন বড়োবাবু আর অশ্রুসংবরণ করতে পারলেন না; তাঁর চোখ দিয়ে, তাঁর নাক দিয়ে দরবিগলিতধারে জল তাঁর দাড়ি চুঁইয়ে তাঁর কম্ফর্টারের অন্তরে প্রবেশ করলে। ফলে সেই গলকম্বলটি ভিজে ন্যাতা হয়ে তাঁর গলায় নেপটে ধরলে। বড়োবাবুর ভ্রম হল যে, কলি তাঁর গলায় গামছা দিয়ে—শুধু গামছা নয়—ভিজে গামছা দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।
৪
ঠিক এই সময়ে একটি জেনানা-বক্স থেকে একটি হাসির আওয়াজ তাঁর কানে এল। সে তো হাসি নয়, হাসির গিটকারি; জলতরঙ্গের তানের মতো সে হাসি থিয়েটারের এক কোণ থেকে আর-এক কোণ পর্যন্ত সাত সুরের বিদ্যুৎ খেলিয়ে গেল। অভিনয়ের দোষে নলের সজোরে পলায়নটি যে ঈষৎ হাস্যকর ব্যাপার হয়ে উঠেছিল তা যাঁর চোখ আছে তিনিই স্বীকার করতে বাধ্য, কিন্তু সেই হাসিতে বড়োবাবুর মাথায় বজ্রাঘাত হল। তাঁর কানে সে হাসি চিরপরিচিত বলে ঠেকল— এ যে পটেশ্বরীর হাসি! যে অঞ্চল থেকে এই হাসির তরঙ্গ ছুটে এসেছিল, সেই অঞ্চলে মুখ ফিরিয়ে ঘাড় উঁচু করে নিরীক্ষণ করে তিনি দেখলেন যে, চিকের গায়ে মুখ দিয়ে যে বসে আছে, তার দেহের গড়ন ও বসবার ভঙ্গি ঠিক পটেশ্বরীর মতো। অবশ্য চিকের আড়াল থেকে যা দেখা যাচ্ছি, সে হচ্ছে একটি রমণীদেহের অস্পষ্ট ছায়া মাত্র, কারণ সে বক্সের ভিতরে কোনো আলো ছিল না। তাই নিজের মনের সন্দেহ ঘোচাবার জন্য, তাকে একবার ভালো করে দেখে নেবার জন্য বড়োবাবু দাঁড়িয়ে উঠে সেই বক্সের দিকে ফ্যালফ্যাল্ করে চেয়ে রইলেন। এবারও তিনি সে স্ত্রীলোকটির মুখ দেখতে পান নি, তাঁর চোখে পড়েছিল শুধু কালো কস্তাপেড়ে একখানি সাদা সুতোর শাড়ি। বড়োবাবু জানতেন যে, ওরকম শাড়ি তাঁর স্ত্রীরও আছে। এর থেকে তাঁর ধারণা হল যে, ও শাড়ি যার গায়ে আছে সে নির্ঘাত পটেশ্বরী। তার পর তাঁর মনে পড়ে গেল যে, ও শাড়ির ‘আঁচড়ে উজোর সোনা লুকানো আছে। সেই তপ্তকাঞ্চনের আভায় তাঁর চোখ ঝলসে গেল, তার আঁচে তাঁর চোখের তারা দুটি যেন পুড়ে গেল, তিনি চোখ চেয়ে অন্ধকার দেখতে লাগলেন।
ওভাবে দণ্ডায়মান বড়োবাবুকে সম্বোধন করে চার দিক থেকে লোকে ‘sit down’ ‘sit down’ বলে চীৎকার করতে লাগল। তাঁর পাশের ভদ্রলোকটি বললেন, “মশায়, থিয়েটার দেখতে এসেছেন, থিয়েটার দেখুন, মেয়েদের দিকে অমন করে চেয়ে রয়েছেন কেন? আপনি দেখছি অতিশয় অভদ্র লোক!” এই ধমক খেয়ে তিনি বসে পড়লেন। বলা বাহুল্য, তাঁর পক্ষে অভিনয়ে মনোনিবেশ করা আর সম্ভব হল না। তাঁর চোখের উপরে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে যাচ্ছিল, আর বুকের ভিতর কত কি তোলপাড় করছিল, ছটফট করছিল। এক কথায় তাঁর হৃদয়মন্দিরে দক্ষযজ্ঞের অভিনয় শুরু হয়েছিল।
তার পর অভিনয়ের টুকরো-টুকরো যা তাঁর চোখে পড়ছিল, তাতে তিনি আরো কাতর হয়ে পড়লেন, এই মনে করে— কোথায় দময়ন্তী, আর কোথায় পটেশ্বরী! তার পর তাঁর মনে হল যে পটেশ্বরী যদি তাঁর কাছে মিথ্যে কথা বলতে পারে, বিশ্বাসঘাতিনী হতে পারে, তা হলে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের কোন্ স্ত্রীলোকের পাতিব্রত্যে বিশ্বাস করা যেতে পারে? তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন যে, নলদময়ন্তীর কথা মিথ্যা, মহাভারত মিথ্যা, ধর্ম মিথ্যা, নীতি মিথ্যা, সব মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা! — মানুষের কষ্টই হচ্ছে এ পৃথিবীতে একমাত্র সত্য বস্তু। তখন তাঁর কাছে ঐ অভিনয় একটা বীভৎস কাণ্ড হয়ে দাঁড়াল।
এ দিকে তাঁর হাত-পা সব হিম হয়ে এসেছিল, তাঁর মাথা ঘুরছিল, তাঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে অনবরত ঘাম পড়ছিল— অর্থাৎ তাঁর দেহে মূর্ছার পূর্বলক্ষণ সব দেখা দিয়েছিল। তিনি আর ভিতরে থাকতে পারলেন না— থিয়েটার থেকে বেরিয়ে গিয়ে খোলা আকাশের নীচে দাঁড়ালেন। বড়োবাবু উপরে চেয়ে দেখলেন যে, অনন্ত আকাশ জুড়ে অগণ্য নক্ষত্র তাঁর দিকে তাকিয়ে সব চোখ টিপে হাসছে। এ বিশ্ব যে কতদূর নির্মম, কতদূর নিষ্ঠুর, এই প্রথম তিনি তার সাক্ষাৎ পরিচয় পেলেন। তার পর এই আকাশদেশের অসীমতা তাঁর কাছে হঠাৎ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল, এই নীরব নিস্তব্ধ মহাশূন্যের ভিতর দাঁড়িয়ে তাঁর বড়ো একা একা ঠেকতে লাগল; তাঁর মনে হল, এই বিরাট বিশ্বের কি ভিতরে কি বাইরে কোথাও প্রাণ নেই, মন নেই, হৃদয় নেই, দেবতা নেই—যা আছে তা হচ্ছে আগাগোড়া ফাঁকা, আগাগোড়া ফাঁকি। সেইসঙ্গে তিনি যেন দিব্য-চক্ষে দেখতে পেলেন যে, ঐ-সব গ্রহ চন্দ্র তারা প্রভৃতি আকাশপ্রদীপগুলো ঐ থিয়েটারের বাতির মতো দুদণ্ড জ্বলে যখন নিবে যাবে তখন সংসার-নাটকের অভিনয় চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে, আর থাকবে শুধু অসীম অনন্ত অখণ্ড অন্ধকার! অমনি ভয়ে তাঁর বুক চেপে ধরলে, তিনি এই অনন্ত বিভীষিকার মূর্তি চোখের আড়াল করবার জন্য থিয়েটারে পুনঃপ্রবেশ করবার সংকল্প করলেন। অমনি তাঁর মনশ্চক্ষু হতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সরে গেল, আর তার জায়গায় পটেশ্বরী এসে দাঁড়ালে। অসংখ্য অপরিচিত অসভ্য ও আমোদপ্রিয় লোকের মধ্যে তাঁর স্ত্রী একা বসে রয়েছে— এই মনে করে তাঁর হৃৎকম্প উপস্থিত হল। তিনি যেন স্পষ্টই দেখতে পেলেন যে, চিকের আবরণ ভেদ করে শত শত লোলুপনেত্রের আরক্তদৃষ্টি পটেশ্বরীর দেহকে স্পর্শ করছে, অঙ্কিত করছে, কলঙ্কিত করছে।
এর পর বড়োবাবুর পক্ষে আর এক মুহূর্তও বাইরে থাকা সম্ভব হল না, তিনি পাগলের মতো ছুটে গিয়ে আবার থিয়েটারের ভিতরে প্রবেশ করলেন। এবার তাঁর আর অভিনয় দেখা হল না; তাঁর চোখের সুমুখে কোত্থেকে যেন একটি ঘন কুয়াশা উঠে এসে চার দিক ঝাপসা করে দিলে। দেখতে না দেখতেই অভিনয় ছায়াবাজি হয়ে দাঁড়াল। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কতক কথা তাঁর কানে ঢুকলেও, তার একটি কথাও তাঁর মনে ঢুকল না। কেননা, সে মনের ভিতর শুধু একটি কথা জাগছিল, উঠছিল, পড়ছিল। যে স্ত্রীলোক খিল্ খিল্ করে হেসে উঠেছিল— সে পটেশ্বরী, কি পটেশ্বরী নয়? এই ভাবনা, এই চিন্তাই তাঁর সমস্ত মনকে অধিকার করে বসেছিল। তিনি বারবার সেই জেনানা-বক্সের দিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন, এবং প্রতিবার তাঁর মনে হল যে, এ পটেশ্বরী না হয়ে আর যায় না। শুধু তাই নয়, তিনি রঙ্গালয়ের অন্দরমহলের যে দিকে দৃষ্টিপাত করলেন— সেই দিকেই দেখলেন পটেশ্বরী বসে আছে। ক্রমে এই দৃশ্য তাঁর কাছে এত অসহ্য হয়ে উঠল যে, তিনি চোখ বুজলেন। তাতেও কোনো ফল হল না। তাঁর বোজা চোখের সুমুখেও পটেশ্বরী এসে উপস্থিত হল; পরনে সেই কালা কস্তাপেড়ে শাড়ি, আর মুখ সেই চিকে ঢাকা। তখন তাঁর জ্ঞান হল যে, তাঁর মনে যে সন্দেহের উদয় হয়েছে তা দূর করতে না পারলে তিনি সত্য সত্যই পাগল হয়ে যাবেন। তাই তিনি শেষটা মন স্থির করলেন যে, থিয়েটার ভাঙবার মুখে, যে দরজা দিয়ে মেয়েরা বেরোয়, সেই দরজার সুমুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন। কেননা একবার সামনাসামনি স্বচক্ষে না দেখলে তাঁর মনের এ সন্দেহ আর কিছুতেই দূর হবে না।
তার পর যা ঘটেছিল তা দু কথায় বলা যায়। থিয়েটার ভাঙবার মিনিট-দশেক পরে থিয়েটারের খিড়কিদরজায় একখানি জুড়িগাড়ি এসে দাঁড়াল। বড়োবাবুর মনে হল, এ তাঁর শ্বশুরবাড়ির গাড়ি—যদিচ কেন যে তা মনে হল, তা তিনি ঠিক বলতে পারতেন না। তার পর তিনটি ভদ্রমহিলা আর একটি দাসী অতি দ্রুতপদে এসে সেই গাড়িতে চড়লে, অমনি সহিস তার কপাট বন্ধ করে দিলে। বড়োবাবু এঁদের কারো মুখ দেখতে পান নি, কেননা সকলেরই মুখ ঘোমটায় ঢাকা ছিল। এই তিনজনের মধ্যে একজন মাথায় পটেশ্বরীর সমান উঁচু; তাই দেখে বড়োবাবু বিদ্যুৎবেগে ছুটে গিয়ে পা-দানের উপর লাফিয়ে উঠে দু হাত দিয়ে জোর করে গাড়ির দরজা ফাঁক করলেন। মেয়েরা সব ভয়ে হাঁউ-মাউ করে চেঁচিয়ে উঠল, আর রাস্তার লোকে সব ‘চোর’ ‘চোর’ বলে চীৎকার করতে লাগল। বড়োবাবু অমনি গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে আরম্ভ করলেন, আর পিছনে অন্তত পঞ্চাশ জন লোক ‘পাহারাওয়ালা’ ‘পাহারাওয়ালা’ বলে হাঁক দিতে দিতে ছুটতে লাগল।
এই ঘোর বিপদে পড়ে বড়োবাবুর বুদ্ধি খুলে গেল। তিনি যেন বিদ্যুতের আলোতে দেখতে পেলেন যে, এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে মাতলামির ভান করা। তাতে নয় দুশো টাকা জরিমানা হবে, কিন্তু গাড়ি চড়াও করে ভদ্রমহিলাকে বে-ইজ্জত করবার চার্জে জেল নিশ্চিত। মদ না খেয়ে মাতলামির অভিনয় করা—যখন দেহের কলকব্জাগুলো সব ঠিক ভাবে গাঁথা থাকে তখন সে দেহকে বাঁকানো চোরানো দোমড়ানো কোঁকড়ানো, অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোকে এক মুহূর্তে জড়ো করা, আর তার পরমুহূর্তে ছড়িয়ে দেওয়া অতিশয় কঠিন এবং কষ্টকর ব্যাপার। কিন্তু হাজার কষ্টকর হলেও আত্মরক্ষার্থে, যতক্ষণ না তিনি পাহারাওয়ালা কর্তৃক ধৃত হন, ততক্ষণ বড়োবাবুকে এই কঠিন পরিশ্রম স্বীকার করতে হয়েছিল। তার পর অজস্র চড়-চাপড় রুলের গুঁতো খেতে খেতে তিনি যখন গারদে গিয়ে হাজির হলেন, তখন রাত প্রায় চারটে বাজে। সেখানে থেকে উদ্ধার পাবার জন্য তিনি শ্বশুরালয়ে সংবাদ পাঠাতে বাধ্য হলেন। ভোর হতে না হতেই তাঁর বড়ো শ্যালক তথায় উপস্থিত হয়ে বেশ দু পয়সা খরচ করে তাঁকে উদ্ধার করে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে গেলেন।
রাস্তায় তিনি বড়োবাবুকে নানারূপ গঞ্জনা দিলেন। তিনি বললেন, “এতদিন শুনে আসছিলুম আমরাই খারাপ লোক, আর তুমি ভালো লোক। ডুবে ডুবে জল খেলে শিবের বাবাও টের পান না, কিন্তু তুমি ভুলে গিয়েছিলে যে, ডুবে ডুবে মদ খেলে পুলিসে টের পায়!”
তার পর তিনি শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হলে, তাঁর সঙ্গে তাঁর শ্বশুর কোনো কথা কইলেন না। শুধু তাঁর ছোটো শ্যালক বললেন, “Beauty and the Beastএর কথা লোকে বইয়ে পড়ে; পটেশ্বরীর কপাল-দোষে আমরা তা বরাবর চোখেই দেখে আসছি। তুমি চরিত্রেও যে beast, এ কথা এতদিন জানতুম না; আমরা ভাবতুম পটের ঘাড়ে বাবা একটা জড়-পদার্থ চাপিয়ে দিয়েছেন।”
তার পর তিনি বাড়ির ভিতর গিয়ে দেখেন, পটেশ্বরী মেজেয় শুয়ে আছে। তার গায়ে একখানিও গহনা নেই, সব মাটিতে ছড়ানো রয়েছে। তার পরনে শুধু একখানা কালো কস্তাপেড়ে সাদা সুতোর শাড়ি। কেঁদে কেঁদে তার চোখ দুটি যেমন লাল হয়েছে, তেমনি ফুলে উঠেছে। সে স্বামীকে দেখে নড়লও না চড়লও না, কথাও কইলে না; মড়ার মতো পড়ে রইল। তাঁর সোনার প্রতিমা ভূঁয়ে লোটাচ্ছে দেখে, সে থিয়েটারে গিয়েছিল কি যায় নি—এ কথা জিজ্ঞাসা করতে বড়োবাবুর আর সাহস হল না। তার পর তিনি যে কোনো দোষে দোষী নন, এবং তাঁর নির্মল চরিত্রে যে কোনোরূপ কলঙ্ক ধরে নি—এই সত্য কথাটাও তিনি মুখ ফুটে বলতে পারলেন না। তিনি বুঝলেন যে, আসল ঘটনাটি যে কি, ইহজীবনে তিনিও তা জানতে পারবেন না, তাঁর স্ত্রীও তা জানতে পারবে না—মধ্যে থেকে তিনি শুধু চিরজীবনের জন্য মিছা অপরাধী হয়ে থাকলেন। ফলে, তিনি মহা অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।
এ গল্পের moral এই যে, পৃথিবীতে ভালো লোকেরই যত মন্দ হয়—এই হচ্ছে ভগবানের বিচার!