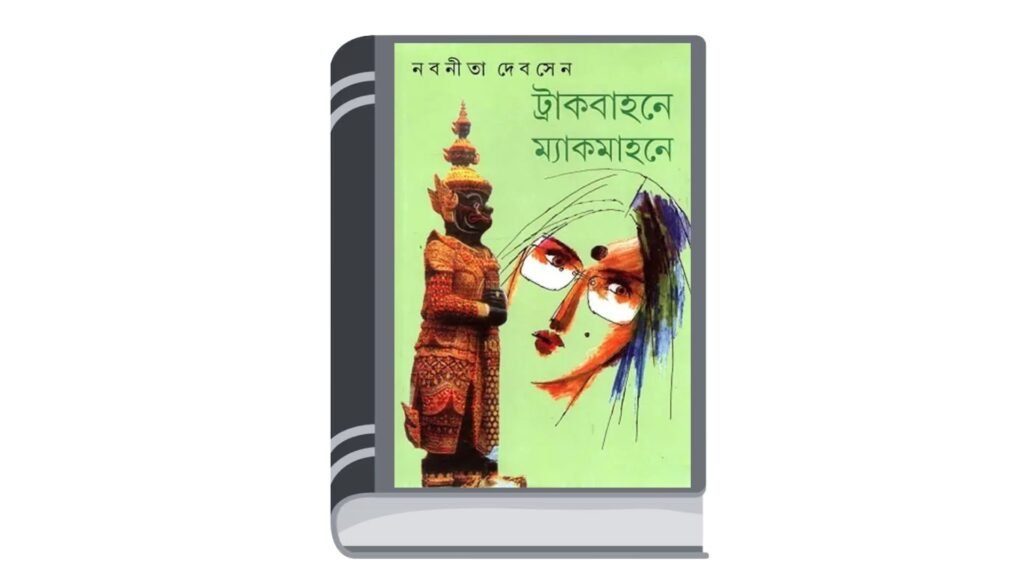ট্রাকবাহনে ম্যাকমাহনে – ১
সভাপর্ব
জোড়হাটের সার্কিট হাউসটি সুন্দর। কিন্তু ঢোকবার মুখে নালার ওপারে সরু সরু শিক লাগানো, এই যা। তার ওপর দিয়ে হেঁটে ঢুকতে একটু অসুবিধা হয়, পায়ে গুডইয়ার কি ডানলপের মতো চওড়া ব্র্যান্ডের জুতো না থাকলে। স্টিলেটো হিল, কি পেনসিল হিল পরি না আমি, আমার তাই পদস্খলনের সম্ভাবনা কম, তবু ভয় ভয় করে। অবশ্য ব্যবস্থাটা হিল পরা মেয়েদের আটকাবার জন্যে ততটা নয় যতটা গোরুদের জন্যে। তারা যাতে বাগানে ঢুকে লাঞ্চ না সারে। দোতলার ঘরে আছি আমি আর নির্মলপ্রভা বরদলৈ। নির্মলপ্রভা সংস্কৃতে ডক্টরেট, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা, এবং বিখ্যাত কবি। তার কিছু লিরিক কবিতা আমি আগেই অনুবাদ করেছি। তার কবিতা গান করেও গাওয়া হয়। আসামে দেখলুম মেয়ে কবিদের মধ্যে এই একটা নতুন ব্যাপার আছে। তারা কবি-কাম-গাইয়ে। প্লাস পণ্ডিত। ডক্টর লক্ষহীরা দাসও গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা, তিনিও কবি, এবং নির্মলপ্রভার মতোই, স্বনামধন্যা গায়িকা। লক্ষহীরা এবং নির্মলপ্রভা সলিল চৌধুরীর মতো নিজের লেখা লিরিকে নিজেরা সুর দেন। তারপর নিজেই গান করেন। সেসব গান হিট হয়। এখানে বহু মেয়েকবি এসেছেন। নীলিমা দত্ত আরেকজন। তিনিও গৌহাটিতে অধ্যাপিকা। জাতে বাঙালি বটে। কিন্তু লেখেন অসমিয়াতে। তাঁর আঠারো বছরের ছেলেটি নকশালি রাজনীতির শিকার হয়েছে—নীলিমাদির কবিতার বইটি তাকেই উৎসর্গ করা। নির্মলপ্রভার লেখায় প্রচণ্ড শক্তির পরিচয় পেয়েছিলুম আগেই। আলাপও হয়েছে আগেই, কলকাতায়। এখানে একঘরে রাত্রিবাস করতে এসে আমাদের বন্ধুত্ব হল। সারারাত্রি না ঘুমিয়ে গল্প করলুম দুজনে। কে বিশ্বাস করবে, এই যুবতী কবির নিজেরও আবার একটি যুবতী কন্যা আছে? সেও ডক্টরেট, সেও অধ্যাপিকা, সেও মা হয়েছে? নির্মলপ্রভার জীবনটাই একটা কিংবদন্তির মতো। শুনতুম আর অবাক হতুম। নির্মলপ্রভা বলেছিলেন তাঁর পরবর্তী প্রেমের কবিতার বই একজন তরুণ বাঙালি কবিকে উৎসর্গ করবেন। করেও ছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে। নির্মলপ্রভা বাদে অন্য অনেকেরই কবিতার সঙ্গে আমার এই প্রথম পরিচয়। আসামে যে এত মহিলাকবি আছেন আমার জানা ছিল না। যে-সব লিটল ম্যাগাজিন থেকে আমি অনুবাদ করেছি, তাতে মেয়েদের লেখা চোখেই পড়ত না বিশেষ। অসমিয়া কবি অনেকের লেখাই আমি আমার সামান্য ভাষাজ্ঞানে, অন্যদের সাহায্য নিয়ে অনুবাদ করেছি। নির্মলপ্রভা, লক্ষহীরা, নবকান্ত বরুয়া, হীরেন গোহাঞি, হীরেন ভট্টাচার্য, হোমেন বরগোহাঞি সকলেরই মৌখিক বাংলা প্রায় নিখুঁত। পরিশুদ্ধ উচ্চারণ, পাকাপোক্ত ভাষাজ্ঞান। আমার বইপড়া অসমিয়া নেহাতই কাঁচা। কষ্টেসৃষ্টে যদিও বা ঠেকেঠুকে পড়তে পারি—বলতে কইতেও পারি না, লিখতেও না। সাধ্য নেই, কিন্তু শখ আছে, অসমিয়া সাহিত্যের ঐশ্বর্যের ভাগ পেতে লোভ যথেষ্ট।
আমার বক্তৃতায় আমি দুঃখ করে বললুম হ্যাঁ, বড়ই লজ্জায় বিষয় যে আমরা বাংলা সাহিত্যের সভায় হিন্দি, ওড়িয়া বা অসমিয়া লেখককে আমন্ত্রণ জানানোর কথা ভাবিই না অথচ আপনারা ভেবেছেন। আমরা ওড়িয়া, হিন্দি, বা অসমিয়া সাহিত্য বিষয়ে অসতর্ক। নিয়মিত খোঁজখবরও রাখি না, ভাষাগুলিও জানি না, যদিও কলকাতায় হিন্দিভাষী ওড়িয়াভাষী অসমিয়াভাষী বাসিন্দার অভাব নেই। অথচ আসামে বসেও আপনারা কী সুন্দর প্রতিবেশীসুলভ উৎসাহে বাংলাসাহিত্য পড়েন। আমি অবিশ্যি এক অসম-প্রেমিক, জাতে বাঙালি, অসমিয়া কবি অমলেন্দু গুহ-র বই “তোমালৈ” আর “লোহিতপারের কথা” পড়বার জন্যে অল্প-স্বল্প অসমিয়া শিখে ফেলে তারপরে কিছু কিছু অন্যান্য কবিদের কবিতাও পড়েছি, অনুবাদও করেছি। কিন্তু আজ এখানে এসে বাংলা সাহিত্যের প্রতি আপনাদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অনুভব করে লজ্জিত এবং অপরাধী বোধ করছি। সত্যিই সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাঙালি এখনও নিজেকে
করে স্বাবলম্বী মনে করে আত্মনিমগ্ন থেকে গেছে। বাংলার বাইরে তার উৎসাহ ছড়াতে পারেনি। তাই, আশাপূর্ণা, সমরেশ, সুনীল, শক্তি বলতেই আপনাদের চোখমুখে যে-আলো জ্বলে উঠছে তার যোগ্য প্রতিবিম্ব আমাদের চোখেমুখে ফোটে না। তবে সুখের বিষয় লিটল ম্যাগাজিনের তরুণ লেখকরা ক্রমশ এই দুর্বলতা বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠছেন, এবং সংশোধনের চেষ্টাও করছেন। অনেক ছোট কাগজে এখন ‘প্রতিবেশী সাহিত্য’ বিভাগ দেখা যাচ্ছে। সুতরাং লক্ষণ শুভ। (এর পরে ‘দেশ’ সাহিত্য সংখ্যায় প্রতিবেশী সাহিত্য আলোচিত হয়েছিল।) আমার কপাল ভাল, বক্তৃতায় সততার অভাব ছিল না বলেই বোধ হয় (এবং দীর্ঘ ছিল না বলেও নিশ্চয়) সকলেই খুব খুশি হলেন। আমি মোটেই বাগ্মী নই, আমার মুখে ঠিক ঠিক কথা জোগায় না কিছুতেই। যদিও অত্যন্ত বকবক করা স্বভাব। মানে, সবচেয়ে খারাপ কম্বিনেশনটা আর কী।
বাগ্মী না হয়েও বাচাল কী করে হওয়া যায়, তারই তাজ্জব প্রমাণ এই শ্রীমতী! যাক, যা হোক করে মাননীয়া প্রধানা অতিথির মান্যগণ্য ভাষণটি তো প্রদত্ত হল। পরন্তু সার্কিট হাউসে ধেয়ে এসে দু-দুজন সাংবাদিক পরপর খুব সিরিয়াস মুখ করে আমার সাক্ষাৎকার পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। প্রথমে পি. কে. বরদলই। মাঝবয়সি “কলা সাংবাদিক” সবার পরিচিত, লেখেন ‘অঘরী’ নামে। আরেকজন তরুণ সাংবাদিক এসেছিলেন রেডিয়ো থেকে। ‘অঘরী’র সঙ্গে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার ‘দৈনিক জনমভূমি’তে বেরিয়েছিল, ‘অঘরী’ তার কাটিং আমাকে পাঠিয়েছিলেন কলকাতায়। শুনলুম রেডিয়োরটা নাকি রেডিয়ো গৌহাটি থেকে প্রচারিত হবে। আমার কিন্তু খেয়াল করে সেটা শোনা হয়নি, কেন না তার আগেই যে জোড়হাট থেকে হাওয়া হয়ে গেছি। যাত্রা শুরু! দুই বোন, আমার দুজন নবীন অসমিয়া বান্ধবী, শ্রীমতী নীতি বরুয়া ও রানী হেনড্রিকে আমাকে যত্ন করে পৌঁছে দিয়েছেন কাজিরাঙ্গার জঙ্গলে, আমার কাজিরাঙ্গা দেখবার শখ ছিল বলে। ওঃ, কী আশ্চর্য সেই বনবাস!
বনপর্ব
—”কাজিরাঙ্গার জঙ্গল না দেখালে কিন্তু সভা করতে যাব না”—এই রকম একটি আহ্লাদে শর্ত করেছিলুম শ্রীমতী শীলা বরঠাকুরের সঙ্গে, যখন তাঁরা আমাকে নেমন্তন্ন করেন ফোনে। তিনি কথা রাখলেন এবং বন্ধুদের সঙ্গে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন কাজিরাঙ্গাতে। টুরিস্ট লজে না রেখে, ওরা আমাকে নিয়ে গেল আশ্চর্য একটি আশ্রয়ে। “কামরূপ কমপ্লেক্স”। এই টুরিস্ট কমপ্লেক্সের তুলনীয় কিছু ভারতবর্ষে এখনও আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। একমাত্র মার্কিন দেশেই দেখেছি এ ধরনের ব্যবস্থা। গাড়ি রাখার বন্দোবস্ত, এবং নানা ধরনের রুচিমাফিক বাসস্থান সেখানে তৈরি আছে—একটা সিংগল হাট নিলুম (কুটিরে থাকার আমার খুব শখ)—একেবারে আশ্রমের প্রান্তে, ছোট নদীটার পাড়ে। এই নদীর ওপারেই কাজিরাঙ্গা ফরেস্ট এরিয়া আর এপাশে সামান্য জনবসতি, গাড়ি চলার বড় রাস্তার ধারে ধারে। নদীটা ছোট হলেও খরস্রোতা। ব্রহ্মপুত্রের সাক্ষাৎ পুত্রী তিনি। যখন তখন বাড়েন-কমেন, বান ডাকেন। তাঁর প্রতাপ বড় কম নয়। ও সব নদীর মেজাজই আলাদা।
“কামরূপ কমপ্লেক্স” শ্রীজগদীশ ফুকন নামে এক চিরতরুণ এক্স জার্নালিস্টের স্বপ্নের ফসল। চাকরি ছেড়ে দিয়ে ছেলেমেয়ে পত্নীসহ তিনি এইখানে এসে জঙ্গলের ধারে নদীর পাড়ে জনবসতির বাইরে অনেকখানি জায়গা জমি নিয়ে নানারকম এক্সপেরিমেন্ট করছেন। বাঁশের মধ্যে চাল মাংস ভরে আকাশের নীচে কাঠের আগুনে ঝলসে আদিবাসী স্টাইলে রেঁধে, বাঁশের গেলাসে আদিবাসী মদ সহকারে শৌখিন বিদেশিদের খাওয়ানোর ব্যবস্থাও যেমন তিনি করতে পারেন, তেমনি আবার মোমের আলোয় লেস দেওয়া টেবিলক্লথে ফরাসি খানা আর বিলিতি মদের ব্যবস্থাও আছে দিশি সায়েবদের জন্যে। দারুণ এক রেস্তরাঁ চালান তাঁরা। আমি সত্যি থ। এত সুন্দর, এত সুপরিকল্পিত (এবং কল্পনাপ্রবণ) শিল্পসম্মত পারিবারিক ব্যবসায় এদেশে আমি আর দেখিনি।
আমার জন্যে পছন্দ করা খোড়ো চালের কুটিরটির ভেতরে চুনকাম করা মাটির দেওয়াল, কিন্তু বাথরুমটি পাকা এবং বিলিতি ব্যবস্থা। কুটিরের সামনে ছোট দাওয়া আছে, তাতে দিব্যি ডেকচেয়ার পেতে বসা যায়। ভেতরে ধবধবে খাট বিছানা, টেবিল-চেয়ার, কুঁজো-গেলাস, ইংরিজি ম্যাগাজিন পর্যন্ত। মোমবাতি, টর্চ, দেশলাই, লণ্ঠন, নানারকম বাতির ব্যবস্থা। হাতপাখাও রাখা হয়েছে। ইস এমনি একটা ঘরে যদি সারা জীবন থাকা যেত? ঐহিক আরামের কোনও গর্ত থেকে সাপ বেরুলে কী করব? শহর কলকাতার মেয়ে, সাপকে ট্যাকল করতে শিখিনি। তা বলে যে বাঘ সিংগিকে ট্যাকল করতে শিখেছি, এমন কথাও বলছি না। তবে হ্যাঁ, জানলা-দরজা ভাল করে বন্ধ করলেই ও সব শত্রুকে এক রকম ট্যাকল করা যায়। কিন্তু সাপ?
শান্তিনিকেতনে ‘প্রতীচী’ বাড়ির বকুলতলায় প্রায়ই সাপ মারা পড়ে বটে, কিন্তু সে সব সর্পশিকারের কৃতিত্ব আমার নয়। আর এটা তো আসামের জঙ্গল! কবি সত্যেন দত্ত যাই বলুন, আমি বাবা সাপের মাথায় নাচি না। সে সব কেষ্টঠাকুরের এরিয়া। আমার হাতপাখা আছে, মশারি আছে, ডেকচেয়ার আছে। মশারিটি বেশ যত্ন করে খাটিয়ে তার ভিতরে হাতপাখা নিয়ে গুটিসুটি শুলেই মনে হয় সকাল পর্যন্ত নিশ্চিন্ত। কিন্তু তার আগে তো বাইরে ডেকচেয়ার পেতে খানিকক্ষণ বসা যাক! সুন্দর রাত। জগদীশ ফুকন, তাঁর স্ত্রী মীরা আর মেয়ে মিতা—তিনজনেরই খুব মনোহর স্বভাব। মীরা ফুকন রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করেন, ঘরদোরগুলি গুছিয়ে রাখেন, রেস্তরাঁটা চালান, সাংসারিক ও গৃহস্থালীর দিক সবটা একাই চমৎকার দেখেন। জগদীশ দেখেন যন্ত্রপাতি, হিসেবপত্তর, ‘বার’-এর ব্যাপার, বাগান, জমিজমা, চাষবাস। মিতার ভাল নাম অর্ঘ্য্যা। সে বাবা-মা দুজনকেই সাহায্য করে। সুসংবদ্ধ, রুচিশীল পরিশ্রমী, শিক্ষিত পরিবার। মা এখনও আশ্চর্য তরুণী, জগদীশও যুবক। মেয়ে কলেজে পড়ছে। ছেলেটি সদ্য গেছে কলকাতায়; চা-কোম্পানিতে জুনিয়র এক্সিক্যুটিভ হয়ে। মা মেয়েকে দুটি বোন মনে হয়। সৃষ্টি কর্তা ধী এবং শ্রী দুটোই দিয়েছেন ঢেলে। জগদীশ কবিতা ভালবাসেন। ইংরিজি, বাংলা, অসমিয়া।
দিন যেটুকু বাকি ছিল, কাটল জগদীশ ফুকনের অর্কিড কালেকশন, তাঁর খেত-খামার বাগান দেখে। চমৎকার একটি জীবন গড়ে নিয়েছেন ওঁরা, দেখলে ঈর্ষা হয়। কয়েকটি গাড়ি আছে, শহরে যাতায়াত করে। বন্দুকও আছে। যদিও জঙ্গলে গিয়ে জন্তু মারার প্রশ্ন ওঠে না, তবে জন্তুরা যদি হঠাৎ ঘরে চলে আসে, তখন অন্য আইন নিতে হবে তো?
কথা রইল সকালবেলায় বনে যাওয়া হবে। মিতাও সঙ্গে যাবে, হাতির পিঠে চড়ে ঘুরব। গণ্ডারই প্রধান দ্রষ্টব্য, হরিণ, বাঘটাগ এক্সট্রা।
কাজিরাঙ্গাপর্ব
ফুকনদের গাড়ি আমাদের নামিয়ে দিল বন-আপিসে, সেখান থেকে গাইড নিয়ে রওনা। প্রথমে নদী পার হতে হবে। একটি ডিঙি বাঁধা আছে। আমাদের গাইডই সেটি চালিয়ে ওপারে নিয়ে গেল। অবশ্য একটি বাচ্চা ছেলেও এল নৌকোয়। সে-ই ফেরত নিয়ে যাবে ডিঙিটা। আমরা নেমে যেতেই নৌকো ফিরে গেল। এখন কেবল বন-জঙ্গল। মিতা, আমি আর বাবরালি। বাবরালির বয়স বেশি নয়, বেশ হাসিখুশি দেখতে। নদীর পাড়টা খাড়াই। আমাদের হাত ধরে টেনে ওপরে তুলে নিলে সে। একটুখানি এগিয়ে খুব উঁচু উঁচু গাছের ঘন সবুজ বন, কত লতায় জড়ানো ঝোপঝাড়, ঠিক ট্রপিকাল ফরেস্ট’ বলতে যা ভাবি, তেমনি। কিন্তু সেটাই পুরো কাজিরাঙ্গা নয়। যা দেখলুম ওই একটুই ওইরকম। বাকিটা দীর্ঘ দীর্ঘ ঘাসে ভরা জলাজমি। ঘন বনের মধ্যে একটুখানি ঘাসজমি পরিষ্কার করা। সেখানেই হাঁটু গেড়ে বসে আছেন, কে? মানসিং। মানসিং এক বিশালবপু দাঁতাল হাতি। একটা দাঁত নেই অবশ্য। একটা মই এনে বাবরালি লাগিয়ে দিল মানসিং-এর পিঠে! সেই মই বেয়ে উঠে পড়লুম অর্ঘ্যা আর আমি। বাবরালিই মাহুত। অর্থাৎ এই বনবিহারে সেই আমাদের ফ্রেন্ড, ফিলসফার অ্যান্ড গাইড। বয়স ত্রিশের মধ্যেই মনে হল, হাসিখুশি ছেলেটি, অর্ঘ্য্যা ওকে চেনে। বাঁধাধরা মাত্র কয়েকজনই মাহুত আছে বনবিভাগের। শ্রীল শ্রীযুক্ত মানসিং উঠে দাঁড়াতেই দেখলুম, বাঃ! উঁচু উঁচু গাছের ডালপালা সব আমার হাতের নাগালে চলে এসেছে। এই বনের সবুজটা কেমন যেন অন্য রকম, কাঁচা রং। যেন গায়ে ঘষলে, হাতে উঠে আসবে।
মানসিং সত্যিই মাননীয় খুবই উঁচু হাতি। ধৃতির কাছে আসামের নানাবিধ হাতির জাতি-প্রকৃতি বিষয়ে বছর দশেক আগে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করেছিলুম। কালার ট্রান্সপেরিন্সি সমেত লেকচার দিয়ে বন্ধুদের হাতিবিশারদ করবার চেষ্টা করেছিলেন ধৃতিকান্ত, কিন্তু এখন কার্যকালে দেখলুম সব ভুলে গেছি। কী এর পিঠের গড়ন? কী বা এর পায়ের ধরন? দাঁতের কায়দা? কপাল? লেজ? খুব চেষ্টা করেও মনে পড়ল না। পড়লে, মাহুতকে একটু ইমপ্রেস করা যেত। হল না। মাহুতই আমাদের ইমপ্রেস করতে শুরু করল। এ বন হচ্ছে তার আজন্ম অধীত শাস্ত্র। এ বিষয়ে অসীম জ্ঞান দেবার ক্ষমতা সে রাখে। হেন প্রশ্ন আমি করতে পারিনি যার উত্তর সে জানে না। অবশ্য গুলতাপ্পিও মেরে থাকলে মারতেই পারে, আমি তো ধরতে পারব না সত্যি না মিথ্যে! তবে আজন্ম এই বনে-জঙ্গলেই বড় হয়েছে বাবরালি, তার বাপ-খুড়োও মাহুত। হাতি নিয়েই তার জীবন, বন নিয়েই তার বাঁচা। গুল মারার দরকার নেই তার। প্রশ্ন করে তার ভাঁড়ার খালি করতে পারি এমন শক্তি আমারই বরং নেই।
আস্তে আস্তে হাতি বন দিয়ে চলল। দুলতে দুলতে ছোট ছোট ডালপালা ভাঙতে ভাঙতে, চিবোতে চিবোতে ছোটখাটো লতাপাতা ছিঁড়তে ছিঁড়তে। এটা চিড়িয়াখানাতে ‘ফুলমালা’র পিঠে চড়া নয়। জঙ্গল প্রথমে ঘন, এবং তারপরে হঠাৎ পাতলা হয়ে গেল। এবার আর অরণ্য নয়, জল-জঙ্গল, বা জংলা-জলা। এত দীর্ঘ ঘাস আমি কোনওদিন দেখিনি। মানসিং-এর ঘাড়-মাথার কেবল ওপরটুকুই বেরিয়ে আছে, বাকিটা এই দীর্ঘ অতিদীর্ঘ, দানবীয় তৃণগুল্মে ঢাকা। আমেরিকান প্রেয়ারিজ আমি দেখিনি, তবে এইরকম ঘাসজমিই হবে বোধ হয়। এ ঘাস নামেই ঘাস। দেখেছি ফ্রান্সে এই ধরনের ঘাসবনে রেজিস্ট্যান্সের সময়ে সৈন্যরা লুকিয়ে থাকত বলে সে ঘাসবনের নামই পালটে গেছে। দক্ষিণ ফ্রান্সে কামার্গ অঞ্চলের মাইলের পর মাইল খোলা ঘাসজমিতে গেছি। সেও জংলা-জলা অঞ্চল। কিন্তু সে-ঘাস, আর এ-ঘাস! সেখানেও খুরের ঘায়ে জল ছুটিয়ে কেশর উড়িয়ে ছুটে যায় ধবধবে সাদা বুনো ঘোড়ার দল, কিন্তু অন্য জিনিস এখানে, বুনো হরিণের ছুটে যাওয়া!
সেখানে খটখটে চাঁদি-ফাটানো, আগুন-ঝরানো, মরুভূমির মতন রোদ্দুর। এখানে মেঘের ডাক, আকাশ অন্ধকার। দু-এক ফোঁটা জল পড়তে শুরু করেছে। সেখানে ছিল খোলা জিপ আর মানুষের তৈরি রাস্তা। এখানে মোটে পথই নেই। পায়ে পায়েই আপন পথ কেটে নিয়েছে বন্য জন্তুরা। মানসিং তার চেনা হাতি-চলা রাস্তা ধরেই চলেছে নিশ্চয়, কিন্তু সামনে বা পিছনে সে-রাস্তার দৃশ্যত কোনও চিহ্ন নেই আমাদের চোখে।—
—”বর্ষা বাদল শুরু হবে। আপনাদের ছাতি নেই। দিদিমণিরা কিছু দেখতেও পাবেন না। ভিজেও যাবেন” বাবরালি বলল।—”তার চেয়ে এই একটু হাতির পিঠে বেড়িয়ে-চেড়িয়ে ফিরে চলুন, আজ আর জন্তুরা বেরোবে না। “
—”বেরুবে না মানে? এখানে তো গুহাটুহা দেখছি না? লুকোবে কোথায়?”
—”মানে বৃষ্টির মধ্যে ভাল দেখা যাবে না দূরের জিনিস। বেশি জীবজন্তু বৃষ্টিতে ভিজে জল খেতেও যাবে না। পাখিরাও উড়ে বেড়াবে না। বাঁদররাও হুটোপুটি করবে না।”
—”না করুক। মোটেই ফিরব না। তিন ঘণ্টা ধরে বন দেখবার কথা। তিন ঘণ্টাই ঘুরব আমরা বনে বনে। “
—”ভিজে ভিজে?”
—”তা বৃষ্টি হলে কী করব? ভিজে ভিজেই।”
—”এই নিন, তা হলে আমার ছাতিটা নিন, আমার ছাতি লাগে না।“
কিন্তু যে বৃষ্টিটা শুরু হল, তার ছাটের কাছে ছাতি এবং হাতি সবই তুশ্চু।
অরণ্যে তমশ্ছায়া
ভিজে জবজবে হাতি থেকে নেমে আমরা নৌকো খুঁজতে থাকি। এর মধ্যেই নদীর জল বেড়ে গেছে! আশ্চর্য! মাহুত চেঁচামেচি করে ওপার থেকে নৌকো এবং মাঝি জোগাড় করে দিল। বৃষ্টির জন্যই বোধ হয় এ পারে কিচ্ছু ছিল না। ফরেস্ট অফিসার নেহাত ভালমানুষ। আমরা ফিরেছি দেখে তিনি খুব নিশ্চিন্ত হলেন। বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন—এই অঝোর ঝরন বৃষ্টি, তার মধ্যেই যে দুটো মেয়ে হাতি চড়ে এতক্ষণ ধরে বনে জঙ্গলে জবরদস্তি ঘুরে বেড়াবে, তিনি এটা ভাবতেই পারেননি, (তা যতই শার্ট পেন্টুলুন পরে যাক না কেন তারা!) আপাদমস্তক চুপচুপে রীতিমতো শীত করছে, যেহেতু মাসটা কার্তিকের মাঝামাঝি, ঠাণ্ডা কনকনে একটা হাওয়াও দিচ্ছে পূর্বজন্মের স্মৃতি অবধি বিদ্ধ করে দিয়ে। উষ্ণ আশ্রয়ের লোভে আমরা ফরেস্ট অফিসেই ঢুকে পড়ি। এখন বাড়ি ফিরি কী উপায়ে? এখান থেকে মাইলখানেক তো হবেই “কামরূপ কমপ্লেক্স”, এই বান-ডাকানো টাইপের বৃষ্টির মধ্যে অতটা পথ হন্টনের প্রশ্ন নেই। একটু চা খেলে হত। একপ্রস্থ শুকনো পোশাক পেলে হত। তার আগে অন্তত একটা তোয়ালে পেলে হত! নানারকম চাওয়া-পাওয়ার ভাবনা এখন মাথার মধ্যে খেলে যাচ্ছে। (এতক্ষণ মাথার ওপরে ছাদটা পর্যন্ত ছিল না। ছাদ পেয়েই তোয়ালে, কত কী!)
–“কী করে যে এই বৃষ্টিতে এতক্ষণ হাতির পিঠে আপনারা?” অফিসের অন্যান্য কর্মীরাও হতভম্ব—”আমরা তো ভেবেছিলুম অনেক আগেই ফিরে আসবেন! সত্যি—”
—”ফিরবেন? বৃষ্টি বাড়ায় আরও আহ্লাদ হচ্ছে তো ডাঃ সেনের! জন্তুরা বৃষ্টিতে সব লুকিয়ে পড়ল, তাই ওঁরও জেদ চাপল তাদের খুঁজতে হবে” অর্ঘ্যা ব্যাখ্যা করে।—”দেখেছেন শেষ অবধি। গণ্ডার গোটা তিনেক, দুটো হাতি, বহু হরিণ, অনেক পাখি, আর”—
—”আর একটা বাঘের টাটকা চরণচিহ্ন”–আমিও না বলে পারি না। —”এর আগে কখনও বুনো বাঘের এত কাছাকাছি যাইনি তো? পায়ের ছাপ ধরে লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে দিয়ে—”
—”সর্বনাশ! ওর মধ্যেই তো—”
—”বাঘ লুকিয়ে থাকে? সেজন্যই তো যাওয়া। নদীর ধার অবধি গেলুম। তারপর আর খুঁজে পেলুম না। হারিয়ে গেল।”
–“বাঁচা গেল।” ফরেস্ট অফিসার বলেন।—”বাঘ কেন ভিজতে যাবে আপনাদের দেখবার উৎসাহে? সে নিশ্চয়ই শেলটার নিয়েছিল।”
আবাল্য দেখে আসছি, ছোট ব্যাপারে, বড় ব্যাপারে আমার মনের কথা শুনে নেবার একটা যন্ত্র ওপরওলার কাছে আছে। নইলে ইতিমধ্যে না-বলতেই শুকনো তোয়ালে এসে যায়? এবং তারপরে গরম গরম ধোঁয়া ওঠা চা-ও? তোয়ালেতে মাথা-মুখ, হাত-পা মুছে ফেলা গেল, চা খেয়ে বুকের ভেতরের স্যাঁতসেতে ভাবটা শুকিয়ে নেওয়া গেল। ফরেস্ট বাংলোতে সব কটি ঘরেই অতিথি। একটি তরুণ পঞ্জাবি পরিবার বেড়াতে এসেছেন, বাবা-মা, শিশুকন্যা, আয়া, ড্রাইভার সমেত। তাঁদের সঙ্গেও গল্প হল একটু। বারান্দায় বসে বৃষ্টি দেখতে দেখতে চা খাচ্ছিলেন তাঁরা। হঠাৎ দেখি একটি প্রাইভেট গাড়ি রওনা হচ্ছে কোথায় যেন। অমনি হাঁ হাঁ করে আমি ঝাঁপিয়ে পড়লুম—”কোনদিকে মশাই? কোনদিকে? যায়ে তো যায়ে কাঁহা?”
—”ওটা নয়, ওটা নয়—ওটা অফিসের গাড়ি নয়”–তাড়াতাড়ি বন-অফিসার হেঁকে উঠলেন—”আমার গাড়ি ফিরে এলেই আপনাদের পৌঁছে দেবে। এটা প্রাইভেট গাড়ি।”—আমার কাছে প্রাইভেট গাড়িই বা কী—আর অফিসের গাড়িই বা কী? আমি কি অফিসার?
—”আরে ওতেই হবে! কাস্ট নো বার! আমিও তো প্রাইভেট সিটিজেনই! অ ড্রাইভার মশাই! অ ড্রাইভার সাহেব, আমাদের একটু নামিয়ে দেবেন গো?”—অসহায় ড্রাইভারটি বারান্দায় বসা সেই পঞ্জাবি ভদ্রলোকের দিকেই প্রশ্নসূচক চাউনি ফেলল। ভদ্রলোক আর কীইবা করেন?—”নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই!” না বললে তাঁর ভদ্রলোক থাকার আর উপায় ছিল না!—বহু ধন্যবাদ জানিয়ে, সহাস্যে হাত পা নেড়ে বিদায় নিয়ে তো দুজনে গাড়ি চেপে ফিরে এলুম। তখনও বৃষ্টি পড়ছে। কামরূপ কমপ্লেক্সে গাড়ি ঢোকার নানা অসুবিধে, দু-একটি খিল-তোলা গেট খোলাতে হয়। বৃষ্টির মধ্যে আর দরোয়ানরা বেরোচ্ছে না! নেমে পড়ে নিজেরাই ছুটে ছুটে গেটের তলা দিয়ে গলে ভিতরে চলে গেলুম, গাড়িকে টা-টা করে দিয়ে। আরেকপ্রস্থ ভিজে যখন ফুকন দম্পতি সকাশে হাস্যমুখে নাচতে নাচতে হাজির হলুম, তাঁরা উদ্বেগে ততক্ষণে ফ্যাকাশে হয়ে এসেছেন। কিন্তু অর্ঘ্যা দারুণ উত্তেজিত। তার এত চেনা এই জঙ্গল, অথচ এত মজা নাকি আর কোনওদিনই হয়নি তার এর আগে। আমার তো হয়ইনি। আমার তো আহ্লাদে গদগদ অবস্থা।
‘চিত্রব্যাঘ্রে’র ‘পদনখ চিহ্ন রেখা’ দেখে আমার যত উত্তেজনা, আস্ত আস্ত তিনখানা গণ্ডার দেখেও ততটা না। দুটো হাতিই চুপচাপ সন্ন্যাসীর মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছিল। যেন শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়েছে। গণ্ডারগুলোও ঠিক তাই। আমাদের দেখেই তারা অবিশ্যি নড়েচড়ে গৃহীর মতো ফুরুত করে পালিয়ে গেল। হাতিরা মোটে নড়লই না, এমনই তাদের কনফিডেন্স। কত রকমের পাখপাখালি, কত বিল, (নাকি ঝিল?) কত ঘাসবন, (নাকি শরবন? ) কত ঝিরঝিরে জংলা নদী (নালা?)। মাত্র ওই একটি জায়গায় একটু ঘন সবুজ আব্রু। উঁচু উঁচু বড় বড় গাছের লতাপাতার বন-জঙ্গল। যেখানে হাতিতে চড়তে হয়। বাকিটা তো খোলামেলা। লম্বা লম্বা ঘাসে ভরা একরের পর একর জলা-জমি। বৃষ্টিতে এক ঝাঁক হরিণ সেই জলের মধ্য দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল। উঁচু ঘাসের ফাঁকে যেন ঢেউয়ের মতো গ্রেসফুল তাদের সেই দৌড়, আর সারিবদ্ধ পায়ের ধাক্কায় মাটি থেকে জলের সাদা ফোয়ারা উঁচু হয়ে লাফিয়ে উঠছিল বৃষ্টির মধ্যে—সে দৃশ্য ভোলবার নয়। বেঢপ মোটা শরীর, বর্মচর্ম পরা খড়গধারী রাইনোসেরাসের রিটায়ার্ড মধ্যযুগীয় যোদ্ধার মতো রুম সং-সাজা চেহারা। অমন গাব্দা-গোব্দা গণ্ডারও যে অমনি চকিতে ঘাসবনে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে, কে জানত? সেও অবিস্মরণীয়।—জীবজন্তুর বন্যতার মধ্যে যে দুর্বার গ্রেস আছে, সেটা বনে না গেলে বুঝতে পারতুম না। হ্যাঁ শহরেও বেড়ালের হাঁটা-চলায়, কুকুরের আড়মোড়া ভাঙায় খুবই জান্তব গ্রেস দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু দ্রুত বেগের মধ্যে নিহিত সেটি, সেই গতির গ্রেসটা তো খোলা বনে না গেলে দেখা যাবে না। একবার কর্ণাটকের এক সংরক্ষিত অরণ্যে, নামটা ঠিক মনে পড়ছে না। (নাগরকোট, কিংবা নাগরকোয়েল জাতীয় হবে,) হাতির পিঠে চড়ে যেতে যেতে ২৫-৩০টা বাইসনের একটা ঝাঁককে অবাক হয়ে যেতে দেখেছিলুম। তাদের সেই বিস্মিত দৃষ্টি, এবং মুহূর্তে ছুটে পালানোর পদধ্বনির বাজনা, এবং সেই আকস্মিক ধুলো ওড়া আর শুকনো পাতা ওড়ার দৃশ্য, আর তারও আগে, তাদের সেই শিং সুদ্ধু মাথা নিচু করে স্থির নিষ্কম্প হয়ে সাদা সাদা ভয়-পাওয়া-রাগ- হওয়া চোখে আমাদের পর্যবেক্ষণ করার ভয়ংকর মুহূর্তটি আমার স্মরণে বিদ্ধ। সেবারে একটা চকিত হলুদ বিদ্যুৎও দেখেছিলুম ঘাসের মধ্যে। কী জানি কী জন্তু, কুকুর না হরিণ? ফরেস্ট অফিসে ফিরে এসে দেখি টিন পেটাতে পেটাতে, জ্বলন্ত মশাল নিয়ে বহু লোক বেরিয়েছে—একটা হলুদ বাঘ এসে একটু আগেই নাকি বন-অফিসের পোষা হরিণটা ধরে নিয়ে গেছে। আমরা সেটাকেই হলুদ বিদ্যুতের মতো আসতে দেখেছিলুম। তখন এক বারও ভাবিনি ওটা বাঘ হতে পারে। অনেক গভীর বনে যদিও বাঘ আছে, কিন্তু তাদের দেখা যায় না”—এটাই শুনেছিলুম। দেখা যাবে হরিণ, নীলগাই, শেয়াল, হাতি—আর ভাগ্যে থাকলে বাইসনের দেখা পেতে পারি। তা সেবারেও আমার ভাগ্য অতিরিক্ত ভাল ছিল, এবারেও। আসামের জঙ্গলে বৃষ্টি পর্যন্ত দেখা হয়ে গেল। সোজা কথা? সবাই অবশ্য বলল বৃষ্টি না পড়লেই ভাল হত। ঢের পাখি উড়ত, বাঁদর বেরোত, ঢের বেশি জীবজন্তু দেখা যেত। তা যাকগে, বেশি জন্তু দিয়ে আমার হবেটা কী? সে তো চিড়িয়াখানাতেই আছে। এমন জংলা “আবহাওয়া সৃষ্টি” করত কে, মেঘ-বিদ্যুৎ আর কলসি থেকে ঢালা জলের মতো মোটা ধারার বুনো বৃষ্টি ছাড়া? এমন সকাল বেলার বাদল আঁধারে, কালো মেঘের গুরু গুরু ডাকের মধ্যে, ঝরঝর ঘোর বর্ষার মধ্যে, মানসিং নামক হস্তীপৃষ্ঠে বনবিহার,—আঃ! এর স্বাদই অন্য!
এখনও অর্ঘ্য্যা আমাকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানায়। আর বৃষ্টির সেই দিনটির কথা উল্লেখ করে। তাইতে টের পাই, দিনটা আমার একলারই অদ্বিতীয় সম্পদ হয়ে নেই। ওতে সত্যিই কোনও জাদু ছিল।
যেমন কথা ছিল, ঠিক শীলা বরঠাকুর স্বামী-পুত্র সমেত গাড়ি নিয়ে এসে পড়লেন।
—”কাজিরাঙ্গা কেমন লাগল? বৃষ্টি হয়ে সব নষ্ট, না?”
—”মোটেই না, মোটেই না! দারুণ লেগেছে! দারুণ!”
—”সত্যি?”
—”কাল রাত্তির তো কেটেছে এক্কেবারে বনদেবী স্টাইলে। বনের পশু পাহারা দিয়ে।”
—”অর্থাৎ?”
—”অর্থাৎ নদীর জল খেতে বন্য জন্তুরা তো আসে রাত্তির বেলায়? অনেক রকমের আশ্চর্য বুনো শব্দ শোনা যায়। রাতপাখির গা কাঁপানো শিস, শেয়াল আর ব্যাং-এর কেত্তন তো আছেই, তার ওপরে পাতার খসখস, দূরে দূরে অজানা জন্তুর গর্জন, তার ওপরে আবার কাল রাত্তিরে কোনও একটা যেন উটকো জানোয়ার মনে হল এপারে চলে এসেছে। আমার কুটিরের দেয়ালে গা ঘষছিল। বাইরের দিকে, নদীর দিকে। ওদিকে জানলা টানলা নেই ভাগ্যিস—তবে স্পষ্ট আওয়াজটা শুনেছি, অনেকক্ষণ। ঘরে বসেই জঙ্গলের স্বাদ মিলেছে। অনেক ধন্যবাদ।”
“হ্যাঁ, সেটা পাবেন। বনের শব্দ শুনতে পাবেন। এটা এখানে প্রায়ই ঘটে। সম্ভবত আপনার কপালে গণ্ডারই এসেছিল, ওরা খুব গা ঘষে। ভয়ের কিছু নেই কিন্তু,—ভয়টয় পেয়েছিলেন নাকি? জীবজন্তু এসে আমাদের এই কটেজগুলোর দেয়ালে প্রায়ই গা ঘষে যায়। আমারই বলে দেওয়া উচিত ছিল। ভয় পাননি তো? বেরোবার চেষ্টা করেননি তো?”
—”না না, পাগল? বেরুব কেন? আমার অবিশ্যি তেমন জঙ্গলে ঘোরা অভ্যেস নেই, কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়ায় ছাত্রজীবনে একবার ইওসেমিটি ন্যাশনাল পার্কের জঙ্গলে ক্যাম্পিং করেছিলুম। রাত্তির বেলা ভাল্লুক এসে আমার তাঁবুর গায়ে গা ঘষেছিল, আর ময়লার টিন হাতড়ে এঁটো খাবার দাবার খেয়ে গিয়েছিল। আমি আরেকটু হলেই উল্লাসের চোটে তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়ছিলুম ভাল্লুক দেখতে। আমার বান্ধবী আমার হাত টেনে ধরে আটকে রেখেছিল, বলেছিল, এমনিতে কিছু না করলেও, গ্রিজলি বেয়ার নাকি তেমন লোক ভাল নয়।”
—”বুনোজন্তুকে বিশ্বাস নেই। কখন কী করে!
“এমন চমৎকার জঙ্গলের শব্দের মধ্যে আমার জীবনে একলা একলা রাত কাটল এই প্রথম। ভাগ্যিস জানোয়ারটি এসেছিল, ওর কাছে আমার তো কৃতজ্ঞ থাকা উচিত!”
—”অর্ঘ্যাকে এখানে শুতে বললেই হত।”
–“কী আশ্চর্য, আমার সত্যিই কোনও অসুবিধা হয়নি। ভয় করেনি। একটুও না।” সাহিত্যের বই, কবিতার বই ওখানে প্রচুর। জগদীশ ফুকন কলকাতায় আমাদের বন্ধু হামদি-বে, আর নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীরও বন্ধু। তাঁদের নিমন্ত্রণ পাঠালেন। আর আমাকে বললেন যখনই লেখার জন্য বিশ্রাম এবং নির্জনতা দরকার হবে “কাজিরাঙ্গা ই”-এর উষ্ণ আতিথ্য আমার জন্য সব সময়ে খোলা।
—”অত টাকা কোথায় পাব মশাই? এখানে নিজের খরচে থাকা আমার সাধ্যি নয়”-
—”পয়সা দিতে কে বলেছে? আপনার কলম দিয়ে ভাল একটি লেখা বেরোলেই আমরা মনে করব সব পাওনা মিটে গেল—” ধমকে উঠলেন জগদীশ।—”আতিথেয়তা মানে আতিথেয়তাই। আমরা একা একা বনে-জঙ্গলে পড়ে আছি। সহমর্মী বন্ধু পেলে খুশি হই। চলে আসবেন, যখনই ইচ্ছে করবে। বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে আসার নেমন্তন্ন রইল। নীরেনকে, হামদিকেও বলবেন।”
.
এটা ১৯৭৭, তখনও আসামে বিদেশি বহিষ্করণের কর্মকাণ্ড শুরু হয়নি। তখনও শিল্পপ্রীতিকে ছাড়িয়ে রক্তে ডঙ্কা বাজায়নি রাজনীতি। আমি আসামের যে এক উষ্ণ, প্রেমময়, চেতন, অমানী, শ্রদ্ধেয় মূর্তি দেখে এসেছি, পরে নানাভাবে সেই মূর্তির হানি ঘটিয়েছে সংবাদপত্র আর রেডিয়ো, আসাম থেকে চিঠি, ছাপা পত্রিকায় রিপোর্ট আর উদ্বাস্তু মানুষ আমার দেখা ছবির সঙ্গে পরবর্তী ছবি মেলানো বড় শক্ত।
কিন্তু আমি বিশ্বাস করি শেষ খেলায় মানবিকতাই জেতে। ওটা একটা সাময়িক চিত্তবৈকল্য, রাজনীতির হাতসাফাইয়ের খেলা, ইনডিয়ান রোপ-ট্রিক। ওটা আমাদের আত্মা নয়।
শীলা বরঠাকুর সপতি সপুত্র এবং স-প্রধানঅতিথি সভাশেষ করে ঘরে ফিরছেন। আমাদের গাড়ি গিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদের বুকে একটি ফেরি-স্টিমারে চড়ে বসল। ছটি গাড়ি পরপর চড়তে পারে তাতে। আমরা দোতলায় গিয়ে বসলুম ডেকের ওপর। ঢাকা বারান্দায় চা নিয়ে বসা যায়। যাচ্ছি তেজপুর। শীলা বলেছে তেজপুর না দেখে কেবল জোড়হাট অবধি দেখে ফিরে গেলে সেটা মোটে আসাম দেখাই হল না। আমি তো গৌহাটিতেও যাইনি! ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গেই দেখা হয়নি। তেজপুর উত্তরে, পাহাড়ি অঞ্চলে। সত্যি খুব সুন্দর জায়গা, সবুজ বনপাহাড়ি আছে, ব্রহ্মপুত্র তো আছেই। জোড়হাটের মতো ফ্ল্যাট নয়। বর্ণহীন নয়। আমার অবিশ্যি জোড়হাটও দিব্যি ভাল লেগেছিল। কলকাতার চেয়ে অনেক অন্যরকম তো? অনেক খোলামেলা জায়গা আছে। এক বিজয়-রানী হেনড্রিকের বাড়ির ভেতরেই তো কতখানি জংলা জমি। পুকুরও আছে মনে হল। ধানখেতও চোখে পড়ল। ফুলগাছ, ফুলবাগান তো আছেই। আর বসত বাড়িটাই বা কী আশ্চর্য সুন্দর! বাসগৃহে কাঠ, বাঁশ, বেতের এমন শিল্পসম্মত ব্যবহার রবীন্দ্রনাথ ও রথীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই আসাম ত্রিপুরা থেকেই শিখেছিলেন, মনে হল। আমি যখন যাই তখনও বিজয়ের পিতৃদেব জীবিত ছিলেন। আজ তিনি আর নেই। আছে তাঁর বিপুল গ্রন্থাগারটি তাঁর পাণ্ডিত্যের স্মৃতি নিয়ে।
মহানদ ব্রহ্মপুত্ৰ
ফেরিবোটে চড়ে ব্রহ্মপুত্রের দিকে চেয়ে বুক ভরে গেল। মস্ত নদী। ওপার দেখা যায় না। দূরে দূরে সবুজ সবুজ ফোঁটা, বন-জঙ্গলভরা দ্বীপ ছড়ানো। প্রথমেই মনে হল এমন দ্বীপে-ভরা নদী আগে দেখিনি আমি। হ্যাঁ, দেখেছি তো? জার্মানিতে। রাইন নদীর বুকে অনেক পাহাড়ি দ্বীপ। আর সে সব দ্বীপের বুকে অনেক প্রাচীন দুর্গ। রাইন নদীতে একটা দীর্ঘ নৌকাবিহার করেছিলুম একবার। দ্বীপের বহর আর দুর্গের শোভা দেখে থ হয়ে যেতে হয়। যেন রূপকথার কেল্লা সব। আর ভাগলপুরি গঙ্গার বুকেও অনেক ছোট ছোট পাথুরে দ্বীপ আছে বটে। গৈবীনাথ যেমন একটা, আরও ঢের আছে, আঠারো-উনিশ শতকের সাহেব শিল্পীরা অনেক স্কেচ রেখে গেছেন সেই সব দ্বীপের
কিন্তু বাংলাদেশে দেখিনি তো! আমার এই দুটো চোখ অনেক ঘুরেছে, অনেক দেখেছে। কিন্তু মন প্রথমেই ছোটে কেবল এই বাংলার গণ্ডিটুকুর মধ্যে। ‘বাংলাদেশ’ বলতে আমি পূর্ববঙ্গ বলছি না। এই বিশেষ নামকরণে আমার কিন্তু বুকের ভেতর থেকে একটা হাহাকার আপত্তি হয়ে ওঠে। বাংলাদেশ বলতে বোঝায় সমস্ত বাঙালির জন্মভূমি, যেখানে বাংলা ভাষা বলা হয়—তারপর তার পুব আর পশ্চিম। একটা অংশকে পুরো বাংলাদেশ বলব, আরেকটাকে কেবল পশ্চিমবাংলা, এমন অর্থ-পারম্পর্যহীন লজিকশূন্য নামকরণ জগতে আর কোথাও দেখিনি। কেউ বলে কোরিয়া, নর্থ কোরিয়া? কিংবা ভিয়েতনাম, দক্ষিণ ভিয়েতনাম? কিংবা জার্মানি আর পশ্চিম জার্মানি? কেবল বাঙালির বেলায় আমরা এই সুব্যবস্থা করেছি। নিজেরাই করেছি, নিজেরা মেনেও নিয়েছি। এ নিয়ে কারুর কোনও মনোকষ্ট নেই। আমি ‘বাংলাদেশ’-এর বাসিন্দা নই আর। উদ্বাস্তু না হয়েও বাস্তু থেকে বঞ্চিত হয়েছি। বহুকাল প্রবাসী বাঙালি ছিলুম, ছুটি-ছাটায় আমরা তো বাংলাদেশেই ফিরতুম দিল্লি থেকে। তার মানে ঢাকা-চট্টগ্রামে নয়। কলকাতা-বর্ধমানেও।
যাই হোক, পূর্ববঙ্গের অসামান্য নদী স্বচক্ষে দেখার ভাগ্য এখনও আমার হয়নি, বইতে পড়েছি ‘চর’-এর কথা। চরজাগা ‘দ্বীপ’-এর কথা। তারপরে মনে পড়ল আমাদের সুন্দরবনের মধ্যে প্রচুর দ্বীপ আছে বটে, ব-দ্বীপ। তেমনি এও পলিমাটি জমে তৈরি দ্বীপ। ব্রহ্মপুত্রের বৈশিষ্ট্য এই দ্বীপের কথা মেয়েকে জিওগ্রাফি পড়াতে গিয়ে পড়েছিলুম বটে।
ফেরি ছাড়তে তখনও কিছু দেরি। হাতে সাদা ফুল ছিল। “কামরূপ কমপ্লেক্সের” ফুল। মিসেস ফুকনের দেওয়া। কী মনে হল রেলিঙে ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে একটা ফুল যেই ব্রহ্মপুত্রের স্রোতে ছুড়ে দিয়েছি, চোখের পলকে ফুলটা বহুদূরে চলে গেল! আশ্চর্য তো! এত চওড়া একূল-ওকূল দেখা-না-যাওয়া নদী, তার এমন খর স্রোত? যেন একরত্তি পাহাড়ি ঝর্না?
ওঃ হো, এইজন্যেই তুমি বুঝি নদী নও, নদ? এমন দুর্জয় গতিময়তা, এমন দুর্দান্ত শক্তি আছে বলে? নদী হতে যদি, আরেকটু ধীরস্থির হতে। আরেকটু শান্ত নম্র, আরেকটু ভারভরন্ত চলাফেরা হত! যেমন গঙ্গা, যেমন যমুনা, যেমন গোদাবরী। তবে হ্যাঁ পঞ্চনদ নাম যাই থাক, বাংলায় আমাদের নদের অভাব নেই। শুধু পশ্চিমেই আছেন দামোদর, রূপনারায়ণ, অজয়, দ্বারকেশ্বর, বরাকর। এই তো পাঁচ-পাঁচটি কেউ কেটা। হাঁ করতেই মুখে এসে যায় ক্লাস ওয়ান অফিসার এই পাঁচজনের নাম। কিন্তু তাঁরা কখনও হাঁটুজল, কখনও বুক চিতিয়ে বালির পাঁজরা বের করে, দাঁত ছিরকুটে পড়ে থাকেন, কঙ্কালসার। আবার কখনও সহসা জাগ্রত কুম্ভকর্ণের মতো ধেয়ে আসেন খোলা সুইসগেটের প্রশ্রয় পেয়ে। ভাসিয়ে নিয়ে যান আচমকা গাঁ গঞ্জের জনমানুষ। ব্রহ্মপুত্রও বান ডাকাতে ওস্তাদ, কিন্তু হাঁটুজল—কোমরজল, কিংবা পায়ের পাতা ডোবে না—বালিসর্বস্ব, এমনতর হা-ভাতে ক্লিষ্ট চেহারা তার হয় না কখনও নিশ্চয়। পূর্ববঙ্গের আড়িয়াল খাঁ যেমন, নামটি শুনলেই মনে হয় সেনাপতি। চোখে ক্রোধ, হাতে খোলা তলোয়ার। ব্রহ্মপুত্র শুনলেই মনে হয় মাথার দুধ-সাদা পাগড়িতে বকের পালক গোঁজা, সাদা ঘোড়ায় চড়ে ছুটে চলে যাচ্ছে।
আমার মাথায় কী ঝোঁক চাপল, স্রোতের মধ্যে আবার, আবার ফুল ছুঁড়ে ফেললুম, ব্ৰহ্মপুত্ৰায় মহানদায় নমঃ। আবার আবার ব্রহ্মপুত্র লুফে নিল। মুহূর্তের মধ্যে রিলে হয়ে চলে গেল ওই দূরের দ্বীপের দিকে। এতক্ষণে ফুল নাম্বার ওয়ান হয়তো ওই দ্বীপের পাথুরে কাদায় গিয়ে নোঙর গেড়েছে। বেশ ভাব হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে। চেহারা অতখানি সম্ভ্রান্ত হলে কী হবে বাপু, স্বভাবটা তোমার মোটেই হোমরা-চোমরার মতন ধীরস্থির নয় দেখছি! বিপুল বদন ব্যাঘ্র খৈরি যেমন ছোট রবারের বল নিয়ে খেলা করত, বিপুল বপু ব্রহ্মপুত্রও তেমনি ছোট্ট ফুল নিয়ে খেলছ দেখি আমার সঙ্গে?
জিপবাবু
এক বাঙালি ভদ্রলোকও এই খেয়া নৌকোতে যাচ্ছেন, তাঁর জিপ গাড়ি করে। জিপ গাড়িতে চারিদিকে হলুদ রং ছাপা পর্দা ঝোলানো—আমি তো মুগ্ধ। তারপর দেখি পর্দার ফাঁকে কচিকচি মুখ। স্ত্রী আছেন, বাচ্চারা আছে, তাঁরা সবাই বাংলা বলছেন। বাড়ি কোথায়?—”তেজপুর।”
—”তেজপুরে যাচ্ছেন?”
—”আমরা তেজপুরে উনি বম্ডিলা।”
—”বম্ডিলা?—এই তো আমি খুঁজছি!”
—”তেজপুর থেকে বম্ডিলা কতদূর?”
—”খুব বেশি দূর নয়।”
—”চিনেরা এসেছিল না বমডিলাতে?”
—”ভাগ্যিস তেজপুরে আসেনি?”—শীলা বলে। “তেজপুরে অবশ্য দারুণ ভয় হয়েছিল, “ওই চিনেরা এসে পড়ল” বলে। অনেকেই ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিল।”
—”চিনেরা কিন্তু বম্ডিলা থেকেই ফিরে গিয়েছিল ওই লাসা—তাওয়াং রোড ধরে!” জিপওয়ালা ভদ্রলোক বলেন। —”দারুণ রাস্তা তৈরি করেছিল কিন্তু দশদিনে! এখনও ঠিকঠাক আছে প্রায় কোনও ক্ষতিই হয়নি শুনতে পাই।”
—”তাওয়াং? যেখানে তাওয়াং মনাস্টারি আছে? বম্ডিলা থেকে সেখানে যাওয়ার সোজা রাস্তা না?”
—”হ্যাঁ। তাওয়াং দিয়েই তো ঢুকেছিল চিনেরা। ওইখানেই টিবেট বর্ডার তো, ম্যাকমাহন লাইন।”
শুধু অকারণ পুলকে
—”আচ্ছা, তাওয়াং যেতে হলে কেমন করে যাব জানেন?“
—”কী বললেন? তাওয়াং যাবেন? কেন? হঠাৎ তাওয়াং…? আপনি বুঝি টিবেটান হিস্ট্রি নিয়ে কাজ করছেন? হ্যাঁ, ওখানে ওই বিষয়ে অনেক মেটিরিয়াল পাওয়া যাবে—”
–“–“
—”না? তিব্বতের হিস্ট্রিতে আপনার উৎসাহ নেই? তবে? তাওয়াং? ও, ফিলসফির লোক নিশ্চয়ই। হ্যাঁ, বুদ্ধিস্ট ফিলসফির পক্ষেও—”
–“–“
—”তাও না? হিস্ট্রিও নয়, ফিলসফিও নয়? তবে? দাঁড়ান, বলছি, সিনো-টিবেটান ল্যাঙ্গুয়েজেস?—তাও না?”
এবার ভদ্রলোককে সত্যি উদ্বিগ্ন দেখায়, “তবে কি অ্যানথ্রপলজি? মোপা-খাম্পার দ্বন্দ্ব? ট্রাইবাল কালচার? তাও নয়? অ! এবার বুঝেছি। পলিটিকাল সায়েন্স! বর্ডার ডিসপিউট, ম্যাকমাহান লাইন। এই তো? বলুন, ঠিক ধরেছি কিনা? চাইনিজ অ্যাগ্রেশন, লাসা- তাওয়াং রোড। বম্ডিলা অকুপেশন। টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরিতে মোটামুটি ১৯১৪, ১৯৩৭-৩৮-৩৯, ১৯৫১ আর ১৯৬২–এই ডেটগুলো আপনার জরুরি। হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা তাওয়াং ইজ কোয়াইট ইম্পট্যান্ট, পজিশনালি!”
—”কিন্তু আমি এগুলোর কোনওটা নিয়েই গবেষণা করছি না। মোটে গবেষণাই করছি না তাওয়াং নিয়ে। হঠাৎ খুব ইচ্ছে করছে তাওয়াং যেতে! ১৯৭৫-এ, শিলঙে, একটি দার্শনিক বন্ধুর (রীতা গুপ্ত) কাছে শুনেছিলুম প্রচুর নাকি রেয়ার তিব্বতি পুঁথি আছে ওখানে। কিন্তু খুব দুর্গম পথ। কেউই বিশেষ যায় না। ভেরিয়ের এলুইন অবিশ্যি গেছলেন, কবছর আগে।”
—”মিসেস কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায়ও তো গিয়েছিলেন। গেলে কী হবে? ফিরতে পারেননি।”
—”সে কী কথা? উনি এখন দিল্লিতে নেই?”
—”এখন আছেন হয়তো, তবে অনেকদিন ছিলেন না। তাওয়াং-এ আটকে ছিলেন। বরফ পড়ে, পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পুরো শীতকালই থাকতে হত তাঁকে, যদি না হঠাৎ একজনের হার্ট অ্যাটাক হত।”
—”অ্যাঁ? কার আবার হার্ট অ্যাটাক হল? ওঁর কোনও আত্মীয়র বুঝি?”
—”না না, সে ওঁর কেউ নয়, তাওয়াং-এ পোস্টেড একজন অফিসারের। মিলিটারি হেলিকপ্টারে করে তাঁকে বম্ডিলায় নামানো হল—সেই সঙ্গে কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায়কে। বয়স্কা মহিলা, অত ঘোর ঠাণ্ডায় শেষে তাঁর কিছু হয়ে গেলে—নইলে তো এমনিতে মিলিটারি ভেহিকলে সিবিলিয়ান মেয়েদের রাইড দেওয়া নিষেধ। কিন্তু উনি সরকারি কাজেই গেছলেন তো, ওই আর্টস অ্যান্ড ক্রাফ্টস সেন্টারের ব্যাপারে।”
—”আপনিও তাওয়াং-এ ছিলেন?”
—”না না, আমি কেন মরতে যাব অত শীতে, ওই পাণ্ডববর্জিত জায়গায়? জানেন তো ওটা আবার ট্রি-লাইনের ওপারে? বড় গাছপালা কিস্যু হয় না, পাখিপক্ষী নেই, যাচ্ছেতাই জায়গা মশাই, শখ করে কেউ যায় না। নাথিং টু সি, একসেপ্ট টিবেটান ইয়াকস্ অ্যান্ড বুদ্ধিস্ট মাংকস কেবল চমরীগাইতে আর বৌদ্ধলামাতে ভর্তি। ওই দেখতে আপনি যাবেন? ছোঃ। অবিশ্যি গুম্ফাটা ইন্ডিয়ার বিগেস্ট। ওয়ার্লডে সেকেন্ড বিগেস্ট। সবচেয়ে বড়টা তো লাসায়। ধরমশালরটাই বলুন, লে-র টাই বলুন, সে সব গুম্ফা তাওয়াং-এর চেয়ে ছোট। আর কারুর এত বড় লাইব্রেরি নেই। দু হাজারেরও বেশি পুঁথিপত্র আছে। সোজা কথা? ম্যানাস্ক্রিপ্ট লাইব্রেরি তো? ইভন্ স্বর্ণাক্ষরে লেখা বই ইনক্লুডেড। তবে ও সব বইয়ে আপনাকে হাতও দিতে দেবে না। প্রত্যেকটাকে গাছের বাকলের কাপড়ে জড়িয়ে, দড়ি দিয়ে বেঁধে, তাকে তুলে রাখে। শুনেছি নিয়মিত নামায়, ঝাড়ে পোছে, পরিষ্কার করে। বরফের দেশ তো, হাজার হাজার বছরেও, পোকাও ধরেনি, নষ্টও হয়নি, এত যত্নে রেখেছে। পড়তে অবশ্য কেউই পারে না! অত প্রাচীন তিব্বতি আর কজন জানে? আচ্ছা, আপনি যেতে চান কীসের জন্যে? প্রাচীন তিব্বতি আপনি কি পড়তে পারেন?”
—”পারি না, পারি না। বলছি তো, গবেষণা নয়। নিছক কৌতূহল মাত্র। ‘পাহাড়টা আছে, তাই উঠেছি’ বলার মতন। তাওয়াং-টা আছে, তাই যেতে চাইছি।”
—”তার চে’ গৌহাটি যান না কেন? গৌহাটিও তো আছে। যাওয়াও অনেক সরল, সেফ, এবং গৌহাটিতে প্লেনটি টু সি। কামাখ্যাদেবী দেখেছেন? গৌহাটি ইউনিভার্সিটি? কটন কলেজ?”
—”না। দেখব এখন। আগে তাওয়াং-টা সেরে নিই। তা আপনি তাওয়াং-এর এত খবর রাখলেন কী করে? নিজে যখন যাননি?”
—”বডিলায় আমার অনেকদিন হল তো? বম্ডিলাতে সব খবরই আসে। তাওয়াং অঞ্চল থেকে তো হামেশাই মিলিটারিমেনরা নীচে আসছে। অবশ্য তাওয়াং ইটসেলফ মিলিটারি-ফ্রি এরিয়া, ওই চল্লিশ কিলোমিটারের মধ্যে না ইন্ডিয়ার, না চিনের, কোনও পক্ষেরই মিলিটারি ক্যাম্প থাকতে পারবে না।”
—”বেশ সুব্যবস্থা তো? বর্ডারে গার্ডরা নেই?”
—”আছে। তারা থাকে একদম বর্ডারেই। চিনে আর ভারতীয় সেপাইগুলো নাকি একসঙ্গে খানাপিনা করে। তাওয়াং-এর এদিকে, জাং বলে একটা জায়গায় আমাদের শেষ মিলিটারি ক্যাম্পটি রয়েছে। অর্থাৎ ওপেন ক্যাম্প। সিক্রেট বাংকার্স, আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাম্পস নির্ঘাত আছে তাওয়াং-এ আমাদের। ওপরে কিছু দেখাই যাবে না। সবই সাবটেরানিয়ান ব্যাপার।”
—”সত্যি? ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। এ যে ঘনাদার গল্পের মতন? আরও উৎসাহ হচ্ছে যেতে, বেশ সাবটেরানিয়ান বাংকার্সগুলো দেখে আসব। কখনও তো দেখিনি?”
—”মুণ্ডু দেখবেন। আপনাকে নেমন্তন্ন করে দেখাতে নিয়ে যাবে, না আরও কিছু। টপ-সিক্রেট ও সব। তাওয়াং-য়ের খাস বাসিন্দেরাই এ খবর সাতজন্মে জানে না! আপনি সত্যি কীযে ভেবেছেন জানি না। ওটা খুব সেনসিটিব এরিয়া মশাই। ইনার লাইন পারমিট নিয়েছেন? যাব যাব করে লাফাচ্ছেন যে বড়? পারমিট পারবেন জোগাড় করতে? চেনেন কাউকে?”
—”ইনার লাইন পারমিট? সে আবার কী? কোথায় পাওয়া যায়?”
—”সেটা হচ্ছে ওই রিজার্ভড এরিয়ায় ঢোকার জন্যে সরকারি অনুমতিপত্র অর্থাৎ পাসপোর্ট আর কী, বুঝলেন? অরুণাচলের গভর্নমেন্ট থেকে ইস্যু করে। যাকে তাকে দেয় না। রিজন দেখাতে হবে। ভ্যালিড রিজন।”
—”কোথায় যেতে হবে সেটা নিতে?”
—”ইটানগর। ইটানগর যেতে হবে।”
—”সেটা কোন দিকে? তেজপুর থেকে কতদূরে? বমডিলার পথে পড়বে?”
—”বডিলার উলটো দিকের রাস্তা।”
—”তাই নাকি? এ মা। তবে তো মুশকিল হল। আপনি তো পরশু সকালেই বমডিলা চলে যাবেন।”
—”আমার সঙ্গে আপনার কী?”
–“ভাবছিলুম বম্ডিলা পর্যন্ত যদি আপনার জিপগাড়ি করে যাওয়া যেত।”
–“পারমিট জোগাড় হয়ে গেলে, যেতে পারেন। আপত্তির কিছু নেই তেমন। কিন্তু বম্ডিলায় গিয়ে থাকবেন কোথায়? আমার ওখানে ও সব ব্যবস্থা হবে টবে না। আমার ফ্যামিলি এখন তো থাকছে না ওখানে। ইন্সপেকশন বাংলোতে ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু বম্ডিলাতেই বা যাবেন কেন? দেখবার ওখানে আছেটা কী? সেখান থেকে তো তাওয়াং বহু দূর মশাই। তা ছাড়া তাওয়াং-এ যাচ্ছেন কার সঙ্গে? সঙ্গী জোগাড় করুন আগে। ও সব জায়গায় কখন কী হয়ে যায়, একা একা যাবেন না খবর্দার।”