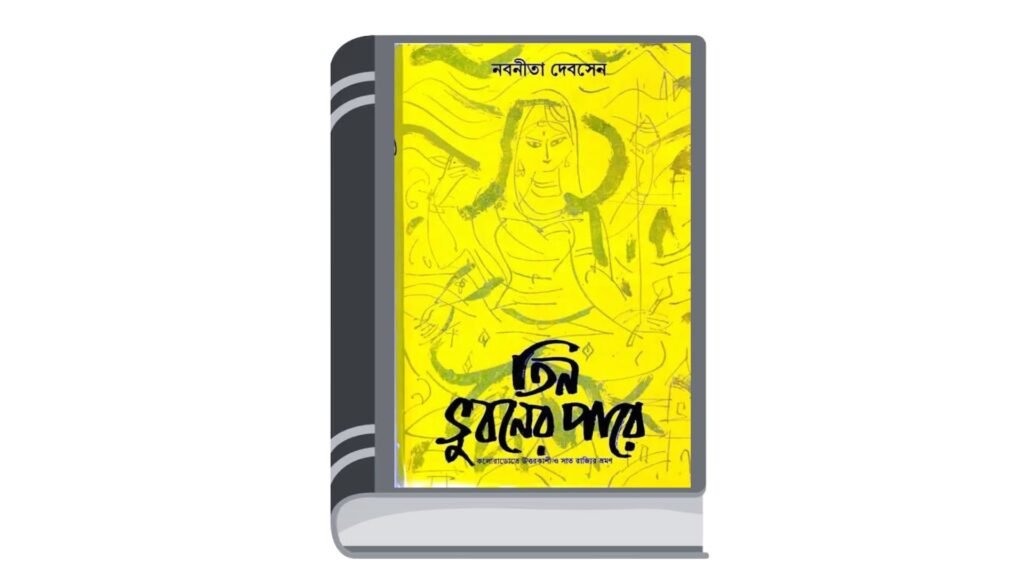আমেরিকার ভারত উৎসব
ভারত-উৎসব ভারত-উৎসব করে থেকে থেকে কত কী শুনি, উৎসুক হয়ে খবরের কাগজে পড়ি, আমার নিজের কপালেও যে ভারত-উৎসবের শিকে ছিঁড়বে তা কখনও ভাবিনি। কিন্তু যখন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভারত উৎসবের সাহিত্য সম্মেলনের আমন্ত্রণ এল, প্রবন্ধ পড়ার এবং কবিতা পড়ার, তখন সত্যি সত্যিই বেজায় উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম। ভেবেছিলাম, এই সুযোগে দিব্যি আমেরিকায় ভারত উৎসবের বিভিন্ন প্রদর্শনী এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের কিছু কিছু দেখবার সুযোগ পাবো। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, নিজের অনুষ্ঠানগুলো ছাড়া ভারত উৎসবের অন্যান্য ব্যাপার-স্যাপার দেখবার কোনও সুযোগই হ’ল না। কিন্তু শিকাগোতে এবং নিউইয়র্কে যে দুটি ভিন্ন প্রতিষ্ঠান আয়োজিত ভিন্ন ধরনের সাহিত্য মিলনসভায় উপস্থিত হতে পেরেছিলাম, অভিজ্ঞতা হিসাবে দুটিই মহার্ঘ হয়ে রয়েছে।
সত্যি বলতে কি, বিদেশ যাওয়া এবং কনফারেন্স করা আমার জীবনে আর কোনও নতুনত্ব আনে না। কিন্তু, এবারের যাত্রার চরিত্র এবং স্বাদ একেবারেই আলাদা। এতদিন ঘোরাফেরা করেছি কেবল পণ্ডিতদেরই সঙ্গে, ওদেশে লেখক-সাহচর্য এই প্রথম। না, কথাটা ঠিক হল না। জেমস্ জয়েস সেন্টিনারিতে ডাবলিন শহরে অকস্মাৎ কয়েকজন রথী-মহারথীর সাহচর্য পেয়ে গিয়েছিলাম। যেন স্বপ্নাদেশে। হোরহে লুইস বোরহেস, অ্যান্টনি বারগেস, বিমুয়া আচিবি, এ সেমবেরগার—এঁরা সকলেই জড়ো হয়েছিলেন ডাবলিনে এক সাহিত্য সেমিনারে নানা খ্যাতিমান জয়েসজ্ঞ পণ্ডিতদের সঙ্গে—আমার সেবারেও ‘স্বপ্ন হল সত্যি’ জাতের অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ছোটবেলাতে বাবা-মায়ের সঙ্গে অবশ্য গেছি ইন্টারন্যাশনাল পি ই এন কংগ্রেসে এডিনবরায়— সেখানেও শুনেছি দেশ-বিদেশের সিদ্ধ সাহিত্যিকেরা এসেছিলেন- কিন্তু আমি তখন বালিকা, তাঁদের সান্নিধ্যের মূল্য বুঝিনি। শিকাগোর বা নিউ ইয়র্কের ব্যাপারটা ঠিক ও ধরনের নয়। বিদেশে যাঁদের সঙ্গে দেখা হল, ভাব জমল, তাঁরা বিদেশী সাহিত্যিক নন, সবাই আমার দেশওয়ালি ভাই। তাই এবারের সাহিত্য সম্মেলনের স্বাদই আলাদা।
শিকাগোতে ভারত-উৎসবের আহ্বায়ক ছিলেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়। কবি-অধ্যাপক এ কে রামানুজনের ব্যবস্থাপনায় ভারতবর্ষ থেকে ৬ জন লেখক এবং পশ্চিমী দুনিয়া থেকে জন ১৫ ভারত বিশারদ অধ্যাপককে এক জায়গায় জড়ো করতে পেয়ে কর্মকর্তারা মহা উল্লসিত। এমন সাড়া পাবেন, তাঁরা ভাবতে পারেননি। সভা শুরুর আগেই, শুধু নিমন্ত্রিতদের তালিকা দেখেই প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস স্বেচ্ছায় প্রবন্ধগুলি প্রকাশ করতে আগ্রহ দেখিয়েছেন, “Your star studded programme” বলে চিঠি দিয়ে।
দেশী লেখক ৬ জনেই কিন্তু টু-ইন-ওয়ান জাতের বস্তু। রামানুজনের পরিপক্ব তামিল ব্রাহ্মণ বুদ্ধিতে তিনি যে ক’জনকেই ডেকেছেন, তাঁরা সাহিত্য সৃষ্টি ছাড়াও প্রায় প্রত্যেকেই ইংরেজির অধ্যাপক, এক গিরিশ কারনাড ছাড়া। তা তিনিও দুর্ধর্ষ রোড স্কলার, অক্সফোর্ডের উজ্জ্বল তারকা। শুধু বোম্বাই-এর রূপোলি পর্দারই নন। তাঁরও দিব্যি গুছিয়ে প্রবন্ধ লেখার ও জমিয়ে বক্তিমে করার অভ্যেস অন্য সকলের মতই আছে। অতএব সকালের সেসনে উপস্থিত অধ্যাপকদের প্রবন্ধের ওপরে সারগর্ভ আলোচনা করে পণ্ডিতদের উত্ত্যক্ত করছি আমরা, দুপুরের সেসনে সেই পণ্ডিত সভায় নিজেরাই প্রবন্ধ পড়ে পণ্ডিতদের মন্তব্য শুনছি, আর সন্ধ্যাবেলা স্বরচিত গল্প-কবিতা-নাটক পাঠে সমবেত জনতার মনোরঞ্জন করছি। সেখানে পাবলিকের প্রবেশ অবাধ। অর্থাৎ একঢিলে বহুপাখি।
গিরিশ স্পষ্টই বললেন—”রামন চালু ব্যক্তি, আমাদের দিয়ে ইন্টেলেকচুয়াল অ্যাক্রোব্যাটিকস্ দেখাবার ব্যবস্থা করেছেন।”
উত্তরে রামানুজন : “এবং তোমরাও তাতে যে কতদূর নিপুণ সেটাই প্রমাণ করেছ—প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমার জয়। প্রত্যেক আমন্ত্রিতই আমার মুখ উজ্জ্বল করেছেন। করবেন। সেটা জেনেই তো ডাকা!”
আমেরিকান পণ্ডিতেরা স্বভাবতই বেশ দাম্ভিক। আমাদের সংস্কৃত পণ্ডিতমশাইদের মতোই, বিনয়ের ধার ধারেন না, সব প্রশংসাই দিব্যি মাথা দুলিয়ে মেনে নেন। আর লেখকদের মধ্যেও বিনয় বস্তুটি সাধারণত অনুপস্থিত। অতএব রামানুজনের এই স্তুতি বাক্যে কেউই চ্যলেঞ্জ করলেন না।
শোনা গেল প্রফেসরের পদের নিচে কাউকে দূর থেকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি বলে মার্কিনী অল্পবয়সী ভারতচর্চাবিদেরা বিরক্ত। শিকাগো এবং তার নিকটবর্তী পাড়ার তরুণ ভারত বিশারদেরা অনেকেই খবর পেয়ে ছুটে গেছেন নিজের খরচে। অবজার্ভার হয়ে। কিন্তু দূরবর্তী অধ্যাপক গবেষকরা সেটা পারেননি, কেননা নিমন্ত্রণের অভাবে পথ খরচা বা ছুটি কোনওটাই যোগাড় করা যায়নি। তা’ সত্ত্বেও সভা জমল দিব্যি। ভারতচর্চা বিষয়ে বিভিন্ন দিক থেকে আলোকপাত করলেন মার্কিনী পণ্ডিতেরা—আর আমরা ছয়জনায় মিলে পথ দেখাই। গিরিশ কারনাড উত্তররামচরিত নিয়ে অসামান্য একটি প্রবন্ধ পড়লেন। তিনি যে এত যত্ন করে সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের চর্চা করেছেন সেটা এদেশেও অনেকেই হয়তো জানেন না, ওদেশে তো জানতেনই না। ফিল্মী ম্যাটিনি আইডলের মডেল অনুযায়ী আমার মনে হ’ল তিনি কোনও ছবিতে একজন সিরিয়াস অ্যাকাডেমিকের ভূমিকায় অসামান্য স্বাভাবিক অভিনয় করছেন। কেবল স্ক্রিপ্টটি তাঁর নিজের তৈরি পেপার। ফিল্মের গুণে গিরিশ কারনাডই ওদেশে সবচেয়ে পরিচিত ও জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব, কিন্তু লেখকদের মধ্যে একবারও তাঁকে তাঁর ‘ফিল্মী ব্যক্তিত্ব’ ব্যবহার করতে দেখা গেল না। সর্বক্ষণ গম্ভীরভাবে পণ্ডিতের মতো এবং লাজুকভাবে তরুণ লেখকের মতো আচরণ করে গেলেন। পোশাকও যেমন-তেমন, কোথাও চোখ ঝলসানোর চেষ্টা নেই, আলাদা হয়ে থাকার চেষ্টা নেই। যদিও তিনি তাঁর রূপ সম্বন্ধে সচেতন, কিন্তু ঐ সভাতে মননশীলতার ঔজ্বল্যই সকলকে মুগ্ধ করেছিল বেশি। গিরিশ প্রায়ই তাঁর পরিবারের, বিশেষত ডাক্তার স্ত্রীর গল্প করেন। শুটিং করতে করতে হঠাৎ চলে এসেছেন, সেমিনার শেষ হলেই ফিরে যাবেন লোকেশনে। একদিনও বেশি থাকতে পারবেন না। তাঁর নানা ভক্ত, অনেকেই এখানে ওখানে নিমন্ত্রণ জানাতে আসছিল। কিন্তু সকলকেই হতাশ করলেন গিরিশ।
একটি গণ্ডির আড়ালে একা প্রায় প্রত্যেকেই। কিন্তু আইয়াপ্পা পানিকরকে তা মনে হয় না। কেরলে একডাকে চেনা নাম। যদি আজকের কেরল থেকে একজনই কবির নাম করতে হয়, তবে তিনি আইয়াপ্পা। মধ্য পঞ্চাশ, একমুখ কাঁচাপাকা গোঁফদাড়ি, একগাল ধবধবে স্বাস্থ্যবান দাঁতের হাসি, কোকড়া চুল, কখনো বুশসার্ট, কখনো পাঞ্জাবি পরা আইয়াপ্পা বেঁটেখাটো মানুষ গলায় সুর আছে, কণ্ঠস্বরটি ভাল। চমৎকার গাইতে পারেন।
তিনি ভারতবর্ষে একলাই একটি তুলনামূলক সাহিত্য প্রয়াসের সংস্থা গড়েছেন। খুব মিশুক, উষ্ণ, বন্ধুবৎসল-স্বভাব। কেরলের প্রবাসীরা এসে তাঁকে রোজই বেজায় টানাটানি করে। কিন্তু পরে নিউইয়র্কে যেমন দেখেছি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে বঙ্গীয় যুবক-যুবতীদের মাতামাতি, তার সঙ্গে অবশ্য তুলনীয় নয় কিছুমাত্র। সুনীলের মক্ষিরানী টাইপের ব্যক্তিত্ব। অবশ্য শুনতে পাই কেরালার মানুষরা বাঙালির মত এমন আবেগপ্রবণ নয়। আইয়াপ্পারও রামানুজন-এর মতো চমৎকার রসিকতাজ্ঞান। কথা বলতে খুব ভাল লাগে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে, যাদবপুরে পক্ষকাল এসেছিলেন অতিথি অধ্যাপক হয়ে। উনি এ বছরের অন্যতম ন্যাশনাল লেকচারার হয়েছেন—ছাত্র-ছাত্রীরা মুগ্ধ, যাবার সময় প্রায় কেঁদেই ফেলে। তারা নানান উপহার দিয়েছিল তাঁকে ভালবেসে। এ থেকেই তাঁর স্বভাবের কিছুটা পরিচয় মিলবে। কেরালা ও দিল্লি—দুই সাহিত্য আকাদেমি থেকেই পুরস্কৃত হয়েছেন তিনি।
আইয়াপ্পার ঠিক বিপরীত নির্মল ভার্মা। নির্মল হিন্দিতে ছোটগল্প লিখে এ বছরে সাহিত্য আকাদেমির পুরস্কার পেয়েছেন। কবি, অধ্যাপকেরা সকলেই আকাদেমি পুরস্কৃত [ অবশ্যই আমি বাদে! ] দেশবাসীর স্বীকৃতিধন্য। নির্মল ছাড়া সকলের লেখার সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ঠতা আছে। আইয়াপ্পার গোটা পঁচিশেক কবিতা তো আমিও অনুবাদ করেছি (কলকাতার ওপরে তাঁর ‘হুগলী’ কবিতা গতবছর একটি শারদীয়াতে যথেষ্ট দৃষ্টি কেড়েছিল)। অনন্তমূর্তির ‘সংস্কার’ উপন্যাস, গিরিশের ‘হয়বদন’ নাটক ছাত্রদের পড়াই, তাঁর ‘তুঘলক’ অভিনয় দেখেছি। নিঃসীম ইজিকিয়েলের (এই বানানটা আমার মনগড়া—Nissim তো বাংলা হয় না।) কবিতা আমার কৈশোর থেকেই পড়ে আসছি—একসময় পি লাল এবং তাঁর নাম ছাড়া ইংরিজিতে কবিতা লেখেন এমন কারুরই নাম শোনা যেত না কলকাতায়। কমলা দাস এলেন তার পরেই। কিন্তু নির্মলের নাম এবং লেখার সঙ্গে দুঃখের বিষয় আমি পরিচিত নই। যদিও পরে টের পেলাম সমসাময়িক হিন্দি গল্পকারদের মধ্যে নির্মল যথেষ্ট জরুরি একজন। নির্মলের স্বভাবটা আমাদের সবার থেকে আলাদা। আমরা প্রত্যেকেই মিশুক—কেবল নির্মল যেমন লাজুক তেমনি একলা। বাঙাল ভাষায় একটা কথা আছে, ‘একাচোরা’। পশ্চিমবঙ্গীয় ভাষার দুটি কথার সমাহার বলে আমার মনে হয় কথাটিকে—একলসেঁড়ে-মুখচোরা। নির্মল এই সমস্তই। তিনি সব সময় পিছিয়ে থাকেন। পারলে হয়তো লুকিয়ে থাকেন। বুফে ডিনারে প্রায় কিছুই খান না। অন্যের বাড়ির খাদ্য স্বহস্তে তুলে নিজেই নিজেকে খেতে দেবেন, এতে বোধ হয় তাঁর সঙ্কোচ। অথচ বহুকাল তিনি ইউরোপে থেকেছেন। ইংলণ্ডে অনেকদিন ছিলেন এবং চেকোস্লোভাকিয়াতে নাকি আটবছর অনুবাদের কাজ করেছেন। দিল্লির এক বিখ্যাত কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে নির্মল এখন স্বাধীনভাবে লিখছেন। তাঁর সংসার নেই।
নিউ ইয়র্কে জন এফ কেনেডি এয়ারপোর্টে লক্ষ করেছি একজন ভারতীয় লোক আমাকে ‘ফলো’ করছে, সেই লণ্ডনের হীথরো থেকে। লাগুয়ারডিয়া এয়ারপোর্টেও শিকাগোর যাত্রীদের লাইনে যখন সে আমারই পিছনে দাঁড়াল, তখন সত্যিই ভয় ভয় করল। লোকটাকে দেখতে অতি নিরীহ। অতি সাধারণ। রোগাসোগা, বেঁটেখাটো, সামনের ক’টা দাঁতও ভাঙা, না পড়ে গেছে কে জানে? রাগ চেপে আমি সাহস করে যেই জিজ্ঞেস করেছি—”আপনি কি আমাকে কিছু বলতে চান?” অমনি একগাল হেসে লোকটা বলল, “হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। আপনি কি নবনীতা? আমি নির্মল ভার্মা। আমরা দুজনেই শিকাগো যাচ্ছি। দিন, আপনার কাঁধের ঝোলাটা আমাকে দিন।” এই হ’ল নির্মল। লাজুক, ভদ্র, পরোপকারী, কিন্তু ইংরিজিতে একটা শব্দ আছে ‘awkward”— ঠিক তাই। আর বাঙাল ভাষাতে নির্মলকে বলবে ‘টলো’। পশ্চিমবাংলায় ওর জন্য কোনও প্রতিশব্দ নেই। এহেন নির্মলের সঙ্গে আমার যে ভাব হবেই বলাবাহুল্য।
২
সাহিত্য সভার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘটল ১৭ এপ্রিল রাত্রে কবি-অধ্যাপক এ কে রামানুজনের বাড়িতে বিশাল নৈশভোজের আমন্ত্রণে। প্রায় ষাটজন উপস্থিত ছিলেন। এই সেমিনারের প্রত্যেক সদস্য। রামানুজন ও আমি একই সঙ্গে প্রথম মার্কিন দেশে ছাত্র হয়ে যাই। আমি সোজা কলেজ থেকে বেরিয়ে, আর রামন দশ বছর কলেজে অধ্যাপনা করার পরে। অক্সফোর্ড বুক অফ ইংলিশ ভার্সেও অনেকদিন ধরেই রামানুজন-এর কবিতা সংকলিত হয়েছে। তিনি নিজে একাধারে কবি এবং পণ্ডিত।
শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারত উৎসবের সাহিত্য সম্মেলন শুরু হ’ল যথাযথভাবে আদি কবিকে নিয়েই। অধ্যাপক রবার্ট গোল্ডম্যান এবং অধ্যাপক শেলডান পোলাক। একদা হার্ভার্ডের দুই ডাকসাইটে সংস্কৃত পণ্ডিত (এখন বার্কলে ও আইওয়াতে অধ্যাপনা করছেন) এক মহৎ কর্মযজ্ঞ শুরু করেছেন। সঠীক বাল্মীকি রামায়ণ অনুবাদের পরিকল্পনা কার্যকরী করেছেন তাঁরা দুজন মিলে। রামায়ণ বিষয়ে দুটি প্রবন্ধ পড়লেন তাঁরা। সভার সভাপতি আলোচক এই শ্রীমতী। আমেরিকার বাঘা বাঘা ভারতচর্চা বিশারদেরা সেখানে উপস্থিত। সংস্কৃতের ওয়েডি ও ফ্লেহারটি, বারবারা স্টোলার মিলার, বাংলার এডওয়ার্ড ডিমক, ক্লিন্ট সীলি, তামিলের জর্জ হার্ট, হিন্দির লিন্ডা হেস, পলিটিক্যাল সায়েন্সের লয়েড ও সুসান রুডলফ, স্বনামধন্য মিলটন ফ্রীডম্যান। অ্যান্থ্রপলজির জোন আর্ডম্যান তো প্রধান ব্যবস্থাপিকা–র্যাল্ফ নিকলসন তখন সেদেশে ছিলেন না, তাঁর স্ত্রী সভায় আসতেন।
১৮ এবং ১৯ দুই সন্ধ্যাবেলায় দুটি সাহিত্যপাঠের আসর বসল। কবিতা পড়ার আসর বসেছিল একটি আধুনিক আর্ট গ্যালারিতে—গল্পপাঠের আসর বসল অন্যত্র। দুটি সন্ধ্যাতেই অসম্ভব ভিড় হল। এত লোক, যে বসার আসন পরিপূর্ণ হয়ে শ্রোতারা দাঁড়িয়ে ছিলেন। কবিতার আসরে বেশ কিছু ভারতীয় মুখ দেখা গেল। দু’তিনজন বাঙালি মেয়ে (সুচরিতা, সুদত্তা, শর্মিষ্ঠা) এবং বেশ কয়েকজন অবাঙালি মেয়ে এবং অবাঙালি ছেলে উপস্থিত ছিলেন। কেবল শিকাগোই নয়, কাছাকাছি কয়েকটা স্টেটের নানান শহর থেকে এমনকী সুদূর আইওয়া সিটি থেকেও গাড়ি-ভর্তি সাত আট জন ছাত্রছাত্রী এসেছিল শিকাগোর সাহিত্য সম্মেলনে অংশ নিতে। কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট, কেউ বুঝি ফিল্ম তৈরি শিখছে, কেউ বা রাইটার্স ওয়ার্কশপে (আইওয়াতে) জার্নালিজমের ছাত্র, কেউ ফিজিক্সের, কেউ লিঙ্গুইস্টিকসের। কেউ তুলনামূলক সাহিত্যের, কেউ অর্থনীতির, কেউ নৃতত্ত্বের। প্রচণ্ড এক মিশ্রণ শ্রোতার দলে। কিন্তু পাঠ্যবিষয় বা কর্মস্থল যার যাই হোক না কেন, সাহিত্য-রুচিতে সবাই একই বিন্দুতে এসে মিশেছে।
প্রথম দিন কবিতা। প্রথমে নিঃসীম ইজিকিয়েল ইংরেজিতে কবিতা পড়লেন। রামানুজন সবাইকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। নিঃসীমই বয়োজ্যেষ্ঠ। তাঁর সব কবিতাই ইংরিজিতে লেখা, তাই তাঁর আর অনুবাদের প্রয়োজন ছিল না। সময় আধ ঘণ্টা। তার মধ্যে মূল এবং অনুবাদ, নিজের খুশিমতো ভাগ করে পড়ার কথা। নিঃসীমের কবিতা খুবই স্মার্ট, কৌতুকপূর্ণ, রঙ্গব্যঙ্গে ঝলমলে সাবলীল। শ্রোতাদের সঙ্গে মুহূর্তেই যোগাযোগ তৈরি হয়। তবে তাঁর ইন্ডিয়ান ইংলিশকে ঠাট্টা করে ৩টি কবিতা ভারতীয়রা যেমন উপভোগ করেছেন, অভারতীয়রা ঠিক তেমনি ধরতে পারেননি মনে হয়। নিঃসীমের পরবর্তী কবি আইয়াপ্পা পানিকর। তিনি পড়লেন প্রথমে মাতৃভাষায়, মালয়ালমে, তারপর তাঁর স্বকৃত অনুবাদে। ইংরিজিতে। পানিকরের গলায় সুর আছে। মালয়ালাম কবিতা তিনি সুরে পড়লেন, চমৎকার গলা। খুবই জমে গেল। অনুবাদও খুব ঝক্ঝকে ইংরেজিতে, যেহেতু পানিকর ইংরেজিরই অধ্যাপক। দেখা গেল উপস্থিত গদ্যকার ও পদ্যকার প্রত্যেকেই ইংরেজির ছাত্র—এক গিরিশ কারনাড ছাড়া। গিরিশ অক্সফোর্ডের রোড স্কলার কিন্তু বিষয়টা তাঁর সাহিত্য ছিল না। পানিকরের কবিতাতেও রঙ্গরসিকতা ব্যঙ্গবিদ্রূপ প্রচুর। হাসতে হাসতে উপচে যেন ফেটে পড়ছিল হলঘর। নিঃসীম ও আইয়াপ্পা দু’জনেই সভা-উজ্জ্বল কবি।
তাঁদের পরে কবিতা পড়তে আমার খুব ভয় করছিল। কেন না আমার কবিতা জনসমক্ষে চেঁচিয়ে পড়বার মতো নয়, নির্জনে বসে একা একা মনে মনে পড়বার। অন্তত যে কটা পড়বো বলে ঠিক করেছি ও অনুবাদ করে এনেছি সেগুলো তো বটেই। ওঁদের পড়া কবিতাগুলির অধিকাংশই ব্যক্তিগত ছিল না। নিঃসীমের ‘কাঁকড়াবিছে’ এবং আইয়াপ্পার একটি ছোট্ট কবিতা ছাড়া। অথচ আমার প্রত্যেকটিই ব্যক্তিগত। লজ্জা ঘেন্না ভয়—কবি সম্মেলনে যোগ দেওয়া—এই তিন থাকতে নয়। অতএব যা থাকে কপালে বলে ভগবানের চরণ শরণ করে কবিতাগুলো পড়েই ফেললুম। প্রথমেই বলে নিলুম যে আমার কবিতার আবহাওয়া একেবারেই ভিন্ন। এরা স্মার্ট কবিতা নয়, ভীতু, লাজুক, অসামাজিক কবিতা। তায় গলাটাও ভাঙা, ঝুরঝুর করছে। প্রথমে বাংলা, পরে স্বকৃত ইংরিজি। ইংরিজি-তে নিজের কবিতা এই প্রথম জনসমক্ষে উপস্থিত করছি। যেহেতু পূর্ববর্তীদের একেবারেই বিপরীতধর্মী, হয়তো সেজন্যই আমার কবিতাও যাকে বলে ছুঁচ-পড়া-নৈঃশব্দ্য তার মধ্যে পড়তে পারা গেল। কাব্য পাঠ অন্তে উপস্থিত সকলকেই সুরায় ও পনীরে, ওয়াইন অ্যান্ড চীজ পার্টিতে অভ্যর্থনা জানালেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়। আর এত প্রশংসা কলকাতায় কবিতা পড়ে কিন্তু কখনো কপালে জোটেনি আমার। আমি তো থ! অনেকেই এসে আমাদের লেখা ইংরিজি কবিতার বই চাইতে লাগলেন। বোঝো ঠেলা! এ যেন স্বপ্ন দেখছি। তবু ভাল যে আইয়াপ্পা ও ইজিকিয়েলের সঙ্গে তাঁদের ইংরিজি বই ছিল। কিন্তু আমার তো এই প্রথম অনুবাদ প্রয়াস। হাতের লেখায় দু’চারটে অনুবাদ মাত্র সম্বল।
পরদিন ১৯এ সন্ধ্যাবেলায় গদ্য পাঠের আসর। প্রথমে অনন্তমূর্তি। “সংস্কার” উপন্যাস আমেরিকার অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই ভারতীয় সাহিত্যের পাঠ্য বই। অনন্তমূর্তি সংস্কারের দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে কিছুটা, এবং শেষ অধ্যায় থেকে কিছুটা পড়লেন। শেষ হতেই বিমুগ্ধ শ্রোতারা হাততালিতে ফেটে পড়লেন। এদিনেও অত্যন্ত ভিড় হয়েছিল। এ ঘরটি ছিল ছোট— বসবার জায়গা ছিল কম, দাঁড়ানোর জায়গা ছিলই না। সেই আর্ট গ্যালারিতেই এটাও করা উচিত ছিল। বসার জায়গা ভরে গিয়েও সেখানে প্রচুর দাঁড়ানোর জায়গা ছিল। চারিদিকে ছিল তরুণ, আধুনিক এক জাপানি চিত্রকরের প্রদর্শনী। আবহাওয়াটা সাহিত্য পাঠের পক্ষে বেশ মনের মতো ছিল।
যাই হোক—সভা খুব জমজমাট হল এখানেও। অনন্তমূর্তির এই লেখাটির সঙ্গে অনেকেই এখানে পরিচিত। তারপর উঠলেন গিরিশ কারনাড। গিরিশের নাটক “হয়বদন” এদের অনেক জায়গায় পাঠ্য এবং গিরিশের মুখখানিও “সংস্কার” “মন্থন” ইত্যাদি সিনেমার কল্যাণে অনেকেরই চেনা। গিরিশ হয়বদনের সূচনাটি কন্নড় ভাষাতে সুরে গেয়ে শোনালেন। খুবই সুরেলা গলা। তারপর সুরুটা একটু কন্নড়ে পড়লেন। তারপর ইংরিজি স্বকৃত অনুবাদ। খুবই অনুগৃহীত বোধ করলেন উপস্থিত শ্রোতারা। কেবল তো নাট্যকারই নয়, একজন অভিনেতাকেও দেখা হলো, শোনা হলো। অনন্তমূর্তির উপন্যাসের অনুবাদ তিনি নিজে করেননি। করেছেন এ কে রামানুজন। তিনিও উপস্থিত ছিলেন। এবং লেখকদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন। এই রকম সুযোগ চট্ করে হয় না। ছবি তো তুললাম। কিন্তু উঠেছে কিনা জানিনা, ফ্ল্যাশ আলো জ্বলেনি। এঁদের পরে নির্মল ভার্মা। যে গল্পটি তিনি বহুক্ষণ ধরে পড়লেন সেটি বিদেশের পটভূমিকায় লেখা। অত্যন্ত সূক্ষ্ম তন্তুর জালে বোনা গল্প। কবিতাধর্মী, অনেকটা চেখভের ধরনের। শান্ত রসের—একলা সুরে গল্প। রাত ১১টা বাজে, সভা ভঙ্গ হ’ল। আবার সুরায় এবং পনীরে গল্পগুজব কিছুক্ষণ। নির্মল জনসভার মুড মেজাজ বুঝতে পারেন না। সত্যিই একক, কবিস্বভাবের। ইজিকিয়েল, পানিকর—এঁদের চেয়ে নির্মল ঢের বেশি বেশি কবিমানুষ।
সভা অন্তে, আমরা ছ’জন লেখক, জুডি, মলি, রামানুজন ও পার্থসারথি—একটা ট্যাভার্নে গিয়ে বসলুম। জুডি হ’ল একজন কবি, মলি রামানুজনের ঔপন্যাসিকা স্ত্রী, আর পার্থসারথি ইংরিজিতে ভারতীয় কবি। অদ্য শেষ রজনী। কাল মধ্যাহ্ন ভোজনে সম্মেলন সমাপ্ত হবে। আমি, গিরিশ, অনন্তমূর্তি আমরা কালই শিকাগো ছেড়ে চলে যাচ্ছি বিভিন্ন দিকে। অনেক রাত্রি পর্যন্ত কবিতা আলোচনা, জীবন বিষয়ক এলোমেলো আড্ডা হল। আমরা সকলেই আছি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল হাউসে। মোটেই আরামপ্রদ ঠাঁই বলব না। তবে সকলে একত্রে থাকার বড়সড় একটা আনন্দ আছে, তাতে ছোটখাটো অসুবিধে আর গায়ে লাগে না।
শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্বের অধ্যাপিকা শ্রীমতী জোন আর্ডম্যানের প্রেমে ও শ্রমে, তাঁর অসাধ্য সাধনের ক্ষমতার ফলেই এই শিকাগো-ভারত-উৎসবটি সম্ভবপর হয়েছিল। এ কে রামানুজনের আমন্ত্রিত জনা বিশেক ভারতজ্ঞ পণ্ডিত ও লেখক প্রত্যেকেই এসে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং সভা সম্পূর্ণ রূপেই সার্থক হয়েছিল বলে নিমন্ত্রণকারীরা সানন্দে জানালেন সভার অন্তে।
বিশে সকালে শেষ সভা। এদিনে ছ’জন লেখক ছ’টি প্রবন্ধ পড়বেন। আমাদের বলা হয়েছে যে যার নিজের সাহিত্যচর্চার অভিজ্ঞতা ও সমকালীন সাহিত্য বিষয়ে প্রবন্ধ লিখবে। কার্যত দেখা গেল প্রত্যেকেই রীতিমতো বিনয়ী ও লাজুক। কেউই নিজের বিষয়ে কিছু লেখেননি। নিঃসীম লিখেছেন ইংরিজি ভাষায় লেখা ভারতীয় সাহিত্য যে ভারতেরই সাহিত্য, সেই বিষয়ে গিরিশ পশ্চিম ভারতের আধুনিক নাট্যচর্চার ইতিহাস নিয়ে মৌখিক বক্তৃতা দিলেন। চমৎকার বললেন। সাধে কি আর অক্সফোর্ডে রোড স্কলার হয়েছিলেন? পানিকর বললেন মালায়লম্ কবিতার সমকালীন চরিত্র নিয়ে। একজন অতি তরুণ কবির কবিতা পড়ে বক্তব্য শেষ করলেন। অনন্তমূর্তি পড়লেন, কন্নড় সাহিত্য ও জীবনে ট্রাডিশন ও মর্ডানিটি নিয়ে খুব সুন্দর প্রবন্ধ আর আমি প্রবন্ধ পড়লুম পঞ্চাশের কবিদের নিয়ে। বাংলা কবিতার কলকাতা-কেন্দ্রিকতা বিষয়ে। কলকাতা যে ভারতবর্ষের আর সমস্ত শহরের চেয়ে একেবারেই আলাদা অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেছে যে জন্যে কলকাতার একটা বিশেষ ঠাঁই আছে বাংলা সাহিত্যে। ঐ সভাতে কবিতার ইংরিজি পড়ে শুনিয়েছি শঙ্খদা, শক্তি ও সুনীলের এবং অলোকরঞ্জন, কবিতাদি প্রণবেন্দু ও তারাপদ’র। (নিজের? nil।) প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ছিল ত্রিশ ও চল্লিশের অগ্রজ কবিদের অবদানের কথা। নীরেনদা, সুভাষদা, অরুণ সরকার।
সভার শেষে অনন্তমূর্তি ও আমি চলে গেলুম আইওয়াতে। নির্মল গেল গ্রিসে। গিরিশ ফিরে এল বম্বে, তার শুটিং আছে। আইয়াপ্পা বার্লিনে। নিঃসীমের সঙ্গেই শুধু আবার দেখা হবে। নিউ ইয়র্কে। মিউজিয়াম অফ্ মডার্ন আর্টে, ৫ই মে, ভারতীয় কবিতাপাঠের আসরে।
৫মে আমি নিউইয়র্কে পৌঁছুলুম। ঐদিনই পড়া। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এসেছেন দুদিন আগেই। আর এসেছেন অরুণ কালোটকর (মারাঠি), কেদারনাথ সিং (হিন্দি), সামসুর রহমান ফারুকী (উর্দু), গোপালকৃষ্ণ আদিগা (কন্নড়), নিঃসীম ইজিকিয়েল (ইংরিজি) এবং আসেননি অমৃতা প্রীতম (পাঞ্জাবি)—তাঁর নাম যদিও আছে পোস্টারে। প্রথমদিনে তাঁর বদলে এ কে রামানুজনকে ডাকা হল প্রাচীন তামিল কবিতার ইংরিজি অনুবাদ পড়তে। এবং নিজের একটি ইংরিজি। মিউজিয়াম অব্ মর্ডান আর্টের কবি সম্মেলনে সুরার গেলাস ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছিল শ্রোতাদের হাতে। এখানেও ঘর ভর্তি হয়ে গিয়ে শ্রোতারা দাঁড়িয়ে ছিলেন। মিউজিয়াম অব্ মর্ডান আর্টের শ্রীমতী লিটা হার্নিক ও তাঁর স্বামী সবাইকে অভ্যর্থনা জানালেন, নিজেদের এবং পোয়েট্রি থারটিন বলে একটি সংস্থার পক্ষ থেকে। তারপর কমিটি ফর ইন্টারন্যাশনাল পোয়েট্রির পক্ষ থেকে বব্ রোজেনথাল সকলকে অভ্যর্থনা জানালেন। এবং তারপরে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে শ্রীঅশোক বাজপেয়ী ধন্যবাদ দিলেন। এবং বারবার বললেন সারা পৃথিবীতে ভারতীয় কবিদের এরকম আন্তর্জাতিক কবিতা পাঠের আসর সঁত্র পঁপিদু বাদ দিলে এই প্রথম। কথাটা কিন্তু ঠিক নয়। তাঁর বোধ হয় ১৫ দিন আগেই শিকাগোয় অনুষ্ঠিত ভারত উৎসবে কবিতা পাঠের আসরের কথাটা জানা ছিল না। কেননা তিনি ওটার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় ছিলেন না। ওটার ব্যবস্থা এই মার্কিন দেশ থেকেই হয়েছে। ভারত উৎসবের পতাকা তলেই। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের চেষ্টায়, এবং সেইটিই প্রথম আসর। MOMA দ্বিতীয়।
৫ মে প্রথম কবিতা পড়লেন একজন মার্কিনি কবিনী, কালো মেয়ে, জেন করটেজ। তাঁর লেখা স্লোগানধর্মী, বড় স্থূল। তাতে কবিতা খুঁজে পেলাম না। শুনলাম তিনি রাগী কবি। পরবর্তী কবি কেদারনাথ সিং। হিন্দিতে পড়লেন ৪টি কবিতা। ইংরিজি অনুবাদ পড়ে দিলেন কমিটি ফর ইন্টারন্যাশনাল পোয়েট্রির একজন তরুণ কবি। তাঁর একটি কবিতা ‘বলদ’ ও তাঁর ছোট মেয়ের উদ্দেশ্যে লেখা একটি কবিতা সবারই খুব ভাল লেগেছিল। তারপর বিরতি। টম উইগেল বলে এক তরুণ মার্কিনি বিরতির পর তাঁর কাব্য পড়লেন। জেন করটেজ স্থূল বিপ্লবী। টম উইগেলের কবিতা স্মার্ট। সূক্ষ্ম রঙ্গরসপূর্ণ। হালকা। রাগীও। তারপরে পড়লুম আমি। আমার কবিতা ছোট। তিনটি বাংলায় ও পাঁচটি পড়লুম ইংরিজিতে। এখানে প্রত্যেকের সময় বিশ মিনিট। আমার পরে বিরতি। অ্যালেন গিনস্বার্গ, সুট টাই পরে নিখুঁত ভদ্রলোক, হাতে চুমু খেলেন। বললেন : অপূর্ব। তক্ষুণি আরেকজনও পাগলা টাইপের লোক এসে খপ্ করে অন্য হাতে চুমু খেয়ে বলল, অপূর্ব। অ্যালেন হেসে বললেন–এর নাম গ্রেগরি করসো, মহান কবি। তিনজনের পুট করে ফটোও তুলে নিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। আরো অনেকে এসে পরিচয় করলেন। বাঙালি মুখ বেশি দেখলুম না—চেনা বলতে করবী নাগ, সুমিত্রা মুখার্জি, বাংলাদেশিনী ফরিদা মজিদ, ইভা ফ্রীডম্যান (প্রায় কলকাতারই মেয়ে) কেরলের মীনা আলেকজান্দার ও রিতা কুণ্ডু—এই তো দেখলুম। আমার পরে পড়লেন ডেভিড র্যাটট্রের। তাঁর পরে এ কে রামানুজন। রামানুজন ইংরিজিতেই পড়লেন। প্রাচীন তামিল কবিতা আবৃত্তি করছিলেন কপালেশ্বর নামে এক তরুণ তামিল ছাত্র।
কেদারনাথ সিং কোনও ভূমিকা দেননি, কিন্তু আমি আমার কবিতা পড়বার আগে অল্প করে দু-চার লাইনে একটু বলে দিচ্ছিলুম কবিতার সূত্র, যাতে বুঝতে সুবিধে হয়। রামানুজনও তাই করলেন। কবিতা খুবই ভালও লাগলো সক্কলের। ধন্য ধন্য প্রশংসা হল ভারতীয় কবিতার। কিন্তু শুনলুম কোনও কাগজ থেকেই কোনও রিপোর্টার আসেনি। টিভি থেকেও নয়। কেবল voice of America-র ডিরেক্টর এসেছেন। বব্ রোজেনথাল দুঃখ করে জানালেন এর আগে ওঁরা হাঙ্গেরিয়ান কবিতার, পোলিশ কবিতার, স্প্যানিশ কবিতার, জাপানি কবিতার সম্মেলন করেছেন—কোনওবারেই নিউইয়র্ক টাইম্স্ লোক পাঠায়নি। টেলিভিশনও নয়। আলাদা করে প্রেস কনফারেন্স ডাকা সত্ত্বেও কভার করেনি। কবিতা পাঠকে ওরা নিউজওয়ার্দি মনে করেন না।
এই সময়ে আমরা যখন নিউইয়র্কে কবিতা পড়ছি, তখনই চেরনোবিলের আণবিক বিস্ফোরণ দুর্ঘটনা ঘটেছে—আর যখন শিকাগোতে কবিতা পড়ছি, তখনই লিবিয়াতে বোমা পড়েছে। শিকাগোতে আমার সর্বক্ষণই লিবিয়ার ব্যাপার এবং নিউইয়র্কে চেরনোবিলের ব্যাপারে মন অস্থির ছিল। কাগজের এক কোণে পড়লুম তালচের-এও নাকি ছোটখাটো একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে আমাদের নিজেদের দেশের আণবিক কারখানায়। একদিন নিউইয়র্ক টাইমসে দুটি চিঠি পড়লুম—তারিখটা মনে পড়ছে না ঠিক— এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে বা মে’র গোড়ায় হবে, এককালীন ভারতে রাষ্ট্রদূত, অধ্যাপক জন কেনেথ গ্যলব্রেথের দীর্ঘ চিঠি, লিবিয়ার বোমার বিষয়ে মার্কিনি, বিশেষত নিউইয়র্ক টাইমসের জঙ্গী মনোভাবের নিন্দে করে। তারই নিচে বেস্ট সেলার লেখক কুট ভনগুটের ছোট্ট চিঠি—”কেন যে ছাই আমাদের মার্কিনিদের মার্কিন দেশের বাইরে পা দিলেই মনে হয় যেন জগৎশুদ্ধ সব্বাই আমাদের ঘেন্না করছে? কেন যে সব্বাই আমাদের এত ঘেন্না করে? আজকের দিনে আমেরিকানরাই পৃথিবীতে সর্বাধিক ঘৃণিত জাতি কেন? আমরা কি কিছু ঘৃণার্হ কাজকর্ম করি?—” ব্যস এইটুকু।
এরই মধ্যে চেরনোবিলের বিস্ফোরণটি যেন আমেরিকার পক্ষে ঈশ্বরদত্ত ঘটনা। লিবিয়া চাপা পড়ে গেল। মার্কিনি কেলেংকারি চাপা পড়ে রুশী কেলেংকারী ওপরে উঠে এল। বিশ্বশুদ্ধ মজে গেল নতুন এক কেচ্ছায়।
এই তো বহির্জগৎ। এর মধ্যেই কবিতা, সুরা, পনীর, মধুময় পৃথিবীর ধুলি। এরই ঠিক মাঝখানে চলেছে ভারত উৎসব। জমজমাট কবিতা পাঠের আসর। বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব। মানব প্রেম সত্যি, বেঁচে থাকাটা আমার মাঝে মাঝে এত অস্বাভাবিক লাগে!
* * *
দ্বিতীয় দিনে মার্কিনি কবিতা পড়লেন ভিক্টর এরনান্দেজ ক্রুজ। মারাঠি কবিতা পড়লেন অরুণ কালোটকর। তিনি চেয়ারে বসে পড়েন। অতীব দুঃসাহসী কবিতা তাঁর, কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়তে লজ্জা করে। অরুণ ইংরেজিতে কবিতা লিখে কমনওয়েল্থ পুরস্কার পেয়েছেন। সামসুর রহমান ফারুকীর উর্দু কবিতা সুরেলা উচ্চারণে বেশ মুশায়রার মতো শোনালো। এঁদের ইংরিজি অনুবাদগুলি তরুণ মার্কিনি কবিরা পড়ে দিচ্ছিলেন—মার্ক, সাইমন, এবং বব ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন। একমাত্র আমিই আমার অনুবাদ নিজে পড়েছি। এদিনই নিঃসীম ইজিকিয়েলও তাঁর কবিতা পড়লেন। এবং বিল জাভাটস্কি। নিঃসীমের ইংরিজি কবিতা মার্কিনি কবিদের কবিতাগুলির চেয়ে ঢের ভাল মনে হল। মার্কিনি তরুণ কবি যাঁদের যোগাড় করা হয়েছিল তাঁরা ঠিক ভারতীয় কবিদের সম-মানের ছিলেন না। দুর্ভাগ্যের বিষয় এবং ক্রোধেরও বিষয় বটে, তলিয়ে ভেবে দেখলে। (হয়তো বা ‘মিউজিয়াম অব্ মর্ডান আর্টের প্রদত্ত সামান্য ২৫০ ডলার দক্ষিণায় বড় বড় কবিরা আসতে রাজি হননি, কে জানে?) নাকি এরা বড় কবিদের ডাকেইনি, অ্যালেনকে ছাড়া? ওস্তাদের মার শেষ দিনে এল। অর্থাৎ তৃতীয় দিনে। জেম্স ল্যাথলিন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, ম্যাগি ডুব্রিস, গোপালকৃষ্ণ আদিগা এবং অ্যালেন গিস্বার্গ। সুনীলের কবিতার প্রীতীশকৃত অনুবাদ খুব সুন্দর করে পড়লেন সুনীলের অনেকদিনের বন্ধু অ্যালেন গিন্স্বার্গ। সুনীলের চারটি কবিতাই বলিষ্ঠ সুনির্বাচিত এবং বাঙালির অতি প্রিয় কবিতা। এদিন অনেক বাঙালিই দূর দূর থেকে এসেছিলেন সুনীলের কবিতা শুনতে। এঁদের কেউ কেউ সুনীলের পূর্ব পরিচিত। আমার সঙ্গেও সকলের চেনা হয়ে গেল। জেমস ল্যাখলিনের কবিতা তেমন কিছু না। কিন্তু ম্যাগি ডুব্রিস, নিউইয়র্কের পথে অ্যাম্বুলেন্স চালান। এই তরুণী শ্বেতাঙ্গিনী কবি অত্যন্ত ভালো কবিতা লেখেন। গোপালকৃষ্ণ আদিগার কবিতা পাঠ এই প্রথম শুনলুম। সত্যি খুব ভাল পড়েন। কবিতাও অনুবাদে যতটুকু বুঝলুম, দুঃসাহসী, তীব্র, তীক্ষ্ণ, তারুণ্যময়। যদিও আদিগা বৃদ্ধ হয়েছেন, স্ত্রীকে সঙ্গে এনেছেন এবং এই তিনদিন লেক্সিং টন হোটেলের ঘরেই শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন। আমাদের কারুরই কবিতা পাঠ শুনতে আসতে পারেননি। এই সুদীর্ঘ উড়নদৌড়ে তাঁর শরীর খারাপ হয়ে পড়েছিল। শ্রোতাদের সুনীল এবং আদিগা দুজনের কবিতা পাঠই খুব ভাল লেগেছে। বিরতির পর অ্যালেন গিবার্গ। প্রথমে ছোট এক ফুট লম্বা একটা হার্মোনিয়াম নিয়ে একটি স্বরচিত গীতি কবিতা গেয়ে শোনালেন তিনি। তারপর আর দুটি কবিতা আবৃত্তি, সবশেষে আরও একটি স্বরচিত গান। অ্যালেনের গলা ভাল, সুর তাল লয়ের জ্ঞান টনটনে। ভারি সুন্দর ব্যালাড গাইলেন। কবিতা সন্ধ্যাটি চমৎকারভাবে শেষ হল। সেই সঙ্গে শেষ হল মিউজিয়ম অব মডার্ন আর্টের কবিতা উৎসব।
কবিতা পাঠের পরে একসঙ্গে সবাই মিলে বাইরে গিয়ে খাওয়া হচ্ছে তিনদিনই। প্ৰথম দিনে চীনে রেস্তারাঁয়, হুননের খাদ্য, আলেন গিনসবার্গ খাওয়ালেন। দ্বিতীয় দিনে ভারতীয় ডিনার, “অন্নপূর্ণায়”, কমিটি ফর ইন্টারন্যাশনাল পোয়েট্রি, খাওয়ালেন। এদিনে ডিনারে এলেন প্রসিদ্ধ বীট কবি গ্যারি স্নাইডার। তিনি স্বয়ং ঐ সময়ে গুগেনহাইম মিউজিয়ামে কবিতা পাঠে এবং “কি করে কবি হলুম” এই বক্তৃতা দিতে ব্যস্ত ছিলেন বলে ভারতীয় কবিতা পাঠে ইচ্ছে সত্ত্বেও আসতে পারেননি। এবং যেতে পারিনি আমরাও। জেমস ও ল্যাখলিনও এদিন সস্ত্রীক এসেছিলেন। উনি অনেকদিন ভারতবর্ষে ছিলেন ফোর্ড ফাউনডেশনের কর্মে। কবিতা পড়লেন অবশ্য তিনি পরের দিন। গ্যারির কাছে আমি কেবলই আলাস্কা বিষয়ে জ্ঞান নিতে লাগলুম, কেননা ভারত ভবনের কবিদের সঙ্গে তো আমার ভ্রমণসূচি নয়। আমি এর পরে হার্ভার্ডে বক্তৃতা দিয়ে চলে যাচ্ছি বেঙ্গল স্টাডিজ কনফারেন্সে। তারপর মিনেসোটার রবীন্দ্র জয়ন্তী, নর্থ ওয়েস্টার্নে রবীন্দ্র জয়ন্তী ও রকফোর্ডে রবীন্দ্র জয়ন্তী সেরে—মেক্সিকো। সেখানে এল কলেহিও ডি মেহিকোয় রবীন্দ্র বক্তৃতা সেরে এবং কবিতা পাঠ করে মেক্সিকো ঘুরে বেড়িয়ে, যাব লস এঞ্জেলেস। তারপরেই বোঁ করে চলে যাচ্ছি আলাস্কা। ইচ্ছে আছে উত্তর মেরু অঞ্চল কিঞ্চিৎ ভ্রমণের, আর্কটিক-ওশ্যান দেখার। জানি না সম্ভব হবে কিনা। কেননা এখানে আমি তিনশো ডলার হারিয়ে ফেলেছি। আর আলাস্কায় ভীষণ পয়সা লাগে। তেলে ভেসে যাচ্ছে ওরা। বড়লোক বেজায়। এবং বিচ্ছিন্ন, সুদূর। জনশূন্য।
২৫শে বৈশাখ নয়—কিন্তু সেদিনটা ছিল ৭ই মে। তৃতীয় দিনের দুপুর বেলায় অ্যালেন গিবার্গের বাড়িতে লাঞ্চের নেমন্তন্ন ভারতীয় কবিদের। ভারি সুন্দর পড়ার ঘর, পুজোর ঘর, বসার ঘর, ছোট্ট ছোট্ট সব। সুন্দর গোছানো। পাড়াটা কিছুটা ইউক্রেনিয়ান, কিছুটা পুয়ের্তোরিকান। রাস্তায় গান হচ্ছে, নাচ হচ্ছে, মারামারি হচ্ছে, প্রেম হচ্ছে, খুন হচ্ছে। অ্যালেনের দোরগোড়ায় গত হপ্তাতেই একজনের মৃতদেহ পড়েছিল। অ্যালেনের ঐ বাড়িতেই তরুণ কবিরা থাকেন। বেশ কয়েকটা ফ্ল্যাটে। যত গাইয়ে বাজিয়ে ছবি আঁকিয়ে আর লিখিয়েদের বাস ঐ ১১, ১২, ১৩ নম্বর রাস্তার পাড়ায়। ডাউনটাউন ম্যানহ্যাটান। অত্যন্ত চমৎকার ভোজ্য—শাকসব্জী, রুটি, ভাত, পনীর, ঠাণ্ডা মাংস, আপেলের রস, আম, তরমুজ, খুরবুজা, কলা, বাদাম, আঙুর। খুব সুন্দর পরিবেশ তৈরি হয়েছিল।
সেন্ট্রাল পার্কে কবিতার আসর বসবে ১০ মে। দুপুরে সুনীলদের নিয়ে শ্রীঅশোক বাজপেয়ী মেরিল্যান্ড থেকে ফিরলেন বেলা বারোটায়। পাঁচজন কবিকে নিয়ে তিনি মেরিল্যান্ডে গিয়েছিলেন কবিতা উৎসবে। কর্মাধ্যক্ষ অশোক নিজেই ছ’নম্বর কবি হয়ে গেছেন নিউইয়র্কের বাইরে গিয়ে। উনি ওখানে নিজের হিন্দি কবিতা এবং ইংরিজি অনুবাদ পড়েছেন। অমৃতা প্রীতমের অনুপস্থিতি একটি শূন্যস্থান সৃষ্টি করেছিল। দু’টোর আগেই আমরা পৌঁছে গেলুম সেন্ট্রাল পার্কে। আমার ভাগ্নে প্রিয়দর্শী অলবানি থেকে এসেছিল একদিনের জন্য, সেন্ট্রাল পার্কে মামীমার কবিতা শুনতে। কলম্বিয়ার Ph.D. ছাত্রী আমার ভাগ্নী উর্মি তাকে ফোন করে বলেছে, “বাবু, রেডিওতে প্রায়ই শুনছি কে এক নবনীতা সেন কবিতা পড়তে এখানে আসছে। মামীমা নয়তো? দেবসেন কিন্তু বলেনি।” বাবু তখন আমার কন্যাকে ফোন করেছে স্মিথ কলেজে এবং নিশ্চিত হয়েছে—যাঁহা সেন, তাঁহাই দেবসেন। এবং তারপরেই হুড়মুড় করে এসে পড়েছে। উর্মিও আসছে সেন্ট্রাল পার্কে। অনেককাল বাদে দেখা হবে।
ট্যাক্সি থেকে নেমে সেন্ট্রাল পার্কে ঢুকছি—প্রায়ই দেখছি ব্যস্ত সমস্ত ভারতীয় মূর্তি সব একদিকে চলেছে। আমি প্রিয়দর্শীকে বলছি চুপি চুপি —”বাবু রে, কবিতা সভার শ্রোতা যাচ্ছে ঐ দ্যাখ!” বাবু কেবল হাসে, আর বলে, “ধুৎ—কত কিছু হচ্ছে আজকে শনিবার সেন্ট্রাল পার্কে!” বহুদিন পরে আজ অত্যন্ত চমৎকার রোদ ঝলমলে শীতশূন্য দিন। বসন্তমলয় পর্যন্ত বইছে। এই কদিন বেশ ককনে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছিল। আজ সেন্ট্রাল পার্কে তো ভিড় হবেই। সবাই বেড়াতে বেরিয়েছে। পার্কে ঢুকে দেখি কোথাও বল গেম হচ্ছে, কোথাও নৌকোর রেস হচ্ছে, কোথাও ছোটদের কীসব প্রতিযোগিতা হচ্ছে, কোথাও ব্যান্ডপার্টির বাদ্য বাজছে, কোথাও পল্লীগীতি গাওয়া হচ্ছে সশব্দে। প্রবল প্রাণ চাঞ্চল্য এবং প্রচণ্ড সাংস্কৃতিক তৎপরতা চতুর্দিকে। দেখি পাজামা-পাঞ্জাবী পরে কাঁধে শাল নিয়ে, চশমা চোখে দাড়িওলা এক তরুণ রবীন্দ্রনাথ জাতীয় চেহারার ভদ্রলোক এক সাহেবের কাছে পথের খোঁজ নিচ্ছেন।—বাবু, এ কিন্তু নির্ঘাৎ কবিরে,—একে ডেকে নে। ওকে ভুল রাস্তায় পাঠিয়ে দিচ্ছে—এ বাঙালি কবি না হয়েই যায় না–বাবু তবুও ডাকতে দিল না। আমাদের তো ব্যবস্থাপকরা ঠিক জায়গায়, Bandshell-এ নিয়ে গেলেন। ৭২ নম্বর রাস্তার কাছে। কলকাতার ৭২ নম্বর বাড়ি থেকে, এখানে ৭২ নম্বর রাস্তা। বেশ চেনাশুনো। সেখানে অনেক শ্রোতা জড়ো হয়েছেন। ৰেঞ্চি সবই ভর্তি। এদিক-ওদিক অনেকে ঘাসেও বসে পড়েছেন। অনেকেই দাঁড়িয়ে। ভারতীয় শ্রোতার সংখ্যা এখানে খুব কম নয়। প্রায় আধাআধি এবং মার্কিন শ্রোতারাও, সেই মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্টের শ্রোতাদের মতোই রীতিমতো ভদ্রলোক—ছেঁড়া খোঁড়া জামাকাপড়ে হিপি-রূপী গাঁজাখোরের মূর্তিধারী শ্রোতা নয়। এদেশের ভারতীয় কাজকর্মে সাধারণত উৎসাহী হয় যারা, তারা দেখি ঐ ধরনের অসামাজিক পংক্তিচ্যুত মানুষ। ফ্রিজ পিপল। অথবা সোজাসুজি অ্যাকাডেমিক। এদের কিন্তু মনে হল কোনওটাই নয়। সাধারণ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত হয় কবিতা-উৎসাহী—নয়ত ভারত-উৎসাহী স্ত্রী-পুরুষ, যাঁরা বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। বয়েসও প্রায় সকলেরই বেশ বেশি বেশি। কিছু তরুণ-তরুণীও ছিলেন অবশ্য। এক শুভ্রকেশী বৃদ্ধা এসে আমাকে বললেন, “তুমি কি তোমার মেয়ের ওপর লেখা কবিতাটি পড়বে, মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্টে যেটা পড়েছিলে? আমি সেই কবিতাটি শুনতেই এসেছি।” কট্টর ব্রিটিশ উচ্চারণে বাক্য-দুটি আমেরিকার সেন্ট্রাল পার্কে দাঁড়িয়ে শুনে এই বাঙালিনী তো হতবাক—অতি চমৎকৃত। সত্যিই এই বৃদ্ধা এসেছেন আমার একটি কবিতা আবার শুনতে?— এটা কি কবিতার জোর না মাতৃত্বের? আমার প্রথম সন্তানের উদ্দেশে লেখা কবিতা “অন্তরা-১” পড়েছিলুম মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্টে। ভদ্রমহিলা তার কথাই বলছেন।— “জানো, আমার যখন প্রথম সন্তান হয়, তখন আমারও ঠিক ওরকম মনে হত। কিন্তু আমি তো কবিতা লিখি না—। তোমার ঐ কবিতা শুনে তাই বড্ড ভাল লেগেছিল। তোমার কি পাবলিশড্ বই আছে?” হা কপাল! বই তো আছে, কিন্তু সে তো তুমি পড়তে পারবে না—সব যে বাংলায়। কিন্তু “অন্তরা-১” কবিতাটি সঙ্গেই আছে—পড়বো বলেই নিয়ে এসেছি, অনুবাদ সহ—ভাগ্যিস! ভদ্রমহিলা তাঁর নাম বললেন শ্রীমতী রে রেমণ্ড। নিউইয়র্কের বাসিন্দা, এশিয়া সোসাইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন।
ভারতীয়দের মধ্যে অধিকাংশই দেখা গেল বঙ্গসন্তান। সামান্য কিছু পাঞ্জাবীও এসেছিলেন। অথচ অমৃতা প্রীতম আসেননি। বিশুদ্ধ মারাঠি, কন্নড়, হিন্দি, উর্দুর শ্রোতা বিশেষ কিন্তু চোখে পড়ল না। সেই সোনালী চশমাধারী শাল কাঁধে পাঞ্জাবী পাজামা ঠিকই একটু পরে সেখানে উপস্থিত হলেন। বাবুকে বললুম—”কিরে? দেখলি?” বাবুটা কেবল হাসে। সে ভদ্রলোক বাঙালি। পরে আলাপ হল। প্রণব রায়। ব্যান্ডস্টান্ডটি পাথর বাঁধানো। স্টেজের অংশটা কিছুটা ঢাকা, সামনেটা খোলা। প্রথমে ঢাকা অংশে মেঝেয় বসে বীণা বাজিয়ে সভা উদ্বোধন করলেন অম্বা দেবী। দক্ষিণী ভদ্রমহিলা। সুন্দর বীণা বাজান। স্টেজে তখন প্রচণ্ড রোদ পড়েছে—স্টেজ পশ্চিমমুখো–শ্রোতারা সূর্যের দিকে পিছন ফিরে বসেছেন ভাগ্যগুণে। কিন্তু কবিতাপাঠক মধ্যাহ্ন সূর্যের মুখোমুখি। শুধু আধ্যাত্মিক নয় শারীরিকভাবেও চ্যালেঞ্জ। চোখ ঝলসে যাচ্ছে। শুরুতে অ্যালেন গিার্গ তাঁর খুদে হার্মোনিয়াম নিয়ে আশ্চর্য এক গীতি-বক্তৃতা দিলেন। তাঁর ভূমিকা, কবিপরিচিতি ও সভার সূচনা সবই তিনি তাৎক্ষণিক সুরে ও শব্দে বানিয়ে বানিয়ে গেয়ে দিলেন। তালের লয়ের বিন্দুমাত্র ছন্দ পতন হল না। অ্যালেনের গানটি অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী হয়েছিল—সুরের জন্যেও শব্দের কারণেও। অ্যালেন বললেন, মার্কিনি কবিরা নানা দেশে গিয়ে কবিতা শুনিয়ে আসে। কিন্তু অন্যদেশের কবিদের কদাচ ডাকে না। আমরা অন্যদের কবিতা শুনতে পাই না’। আমাদের মহা সৌভাগ্য যে ভারতবর্ষের কবিরা আমাদের দেশে পায়ের ধুলো দিয়েছেন এবং এমন সুবর্ণ সুযোগ পাচ্ছি তাঁদের কবিতা শোনার। এখানে কেবলই ভারতীয়দের কবিতা পড়া হবে মাতৃভাষায় এবং ইংরিজিতে। প্রথমেই পড়বেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। শেষকালে পড়বেন জ্যেষ্ঠতম গোপালকৃষ্ণ আদিগা। ঠিক মাঝখানে পড়বো আমি। কি শিকাগো, কি সেন্ট্রাল পার্ক, মেয়ে বলতে আমিই একা কুম্ভ। সুনীলের পর হিন্দি কবি—কেদারনাথ সিং, মারাঠী অরুণ কালোটকর, তারপর আমি। তারপর ঊর্দু ফারুকী, তারপর আদিগা কন্নড। এবং সবশেষে ভারত ভবনের কর্মাধ্যক্ষ, অশোক বাজপেয়ীর হিন্দি কবিতা। অশোক তরুণ কবি হিসেবে হিন্দিতে মধ্যপ্রদেশের ভ্রমণ ও সংস্কৃতির সেক্রেটারি সুপরিচিত নন। কিন্তু ভাল লেখেন। এককালে দিল্লির কলেজে ইংরিজির অধ্যাপকও ছিলেন শুনেছি। সেন্ট্রাল পার্কে ভারতীয় কবিতা খুবই জমলো। প্রচুর মানুষজন। কেউ উঠে চলে গেল না। কেউ শিস দিল না। পচা ডিম কি টোমাটো ছুঁড়লো না। সবাই স্তব্ধ হয়ে মুগ্ধ হয়ে শুনলো। সাহেব মেমরা কি সুন্দর সহ্য করলেন অপরিচিত ভাষার কাব্যপাঠ। তারপর ইংরিজি অনুবাদগুলি পড়ার সময়ে ঠিক ঠিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেল। হাসির জায়গায় হাসি—স্তব্ধতার মুহূর্তে নৈঃশব্দ্য। এবং শেষে প্রচণ্ড হাততালি। এখানেও কবিরা নিজেরা শুধু মাতৃভাষাতেই পড়লেন। এবং একজন করে তরুণ মার্কিনি কবি অনুবাদগুলি পড়ে দিলেন। আমিই কেবল বাংলা আর ইংরিজি দুটোই নিজে নিজে পড়লুম কেন না আমার অনুবাদের পাণ্ডুলিপিতেও এত কাটাকুটি, অন্যে পড়তে পারবে না। তাছাড়া আমার বাংলা মেজাজের গলায় মার্কিনী কণ্ঠস্বর ও সুর ঠিকঠাক শোনাবে কিনা সেই বিষয়েও সন্দেহ ছিল।
সুনীলও কলকাতা বিষয়ে একটি কবিতা পড়েছেন, আমিও কলকাতা বিষয়ে একটি কবিতা পড়েছি এবং উপস্থিত প্রবাসী বাঙালিদের সেগুলি খুবই হৃদয়স্পর্শী হয়েছিল শুনেছি। কিন্তু যাঁরা বাঙালি নন, তাঁদেরও ভাল লেগেছিল। সেন্ট্রাল পার্কে সুনীল পড়লেন মাত্র তিনটিই, বড় কবিতা। কলকাতা ও আমি, হিমযুগ, অসুখের ছড়া। অন্যরা সবাই চার-পাঁচটি। কেবল উর্দু কবি অগুনতি কবিতা পড়লেন বলে মনে হল। আমি ছোট ছোট পাঁচটা কবিতা পড়লুম। কত লোকই যে এসে আমাদের বলেছেন, “খুব ভাল লাগলো।” বেশ কয়েকজন বঙ্গসন্তান বল্লেন—”এতদূরে সেন্ট্রাল পার্কে বসে স্বচক্ষে স্বকর্ণে দেখছি শুনছি সুনীল গাঙ্গুলি দাঁড়িয়ে কবিতা পড়ছেন, এ যেন স্বপ্ন দেখছি। বিশ্বাস হয় না, এত থ্রিলিং।” কেউ বললেন, “একটা ছোটখাটো কলকাতাই যেন আজ সেন্ট্রাল পার্কে উঠে এসেছে—।” নিউইয়র্ক, নিউ জার্সি, এমনকী কানেটিকাট, ম্যাসাচুসেট্স্ থেকেও বাঙালিরা এসেছেন। রেডিওর বিজ্ঞাপন, ও প্রভূত পোস্টারের ফল পাওয়া গেছে।
পরে বস্টনে পুরন্দর দাশগুপ্ত বলে একজনের সঙ্গে দেখা হল। তিনি বললেন, সেন্টাল পার্কের পুলিশরা পর্যন্ত সেদিন খুব মজা পেয়েছিল। দেরি হয়েছিল তাঁর আসতে। ভারতীয়দের কবিতা পড়ার ঠাঁই নিয়ে প্রশ্ন করতেই মহা উৎসাহে দেখিয়ে দিল এবং বলল —”খুব ইন্টারেস্টিং হবে বলে মনে হচ্ছে। বহু লোক জমেছে। আমিও যাব শুরু হলে।” ছিলও বেশ কিছু পুলিশ এদিকে ওদিকে। কিন্তু কবিতা শ্রবণ ভিন্ন তাদের আর কিছুই কর্তব্য ছিল না। না গাঁট কেটেছে কেউ কারুর, না গলা কেটেছে। না বোমা মেরেছে। বাঙালি-মার্কিনি সবাই একবাক্যে জানালেন এটা একটা মুল্যবান ঐতিহাসিক মুহূর্ত—এমনটি আগে কোনওদিন ঘটেনি। সেন্ট্রাল পার্কের ব্যাণ্ডস্ট্যান্ডে জোরাল মাইক লাগিয়ে সূর্যের দিকে মুখ করে ভারতীয় কবিরা যে যার নিজস্ব ভাষাতে কবিতা পড়ে যাচ্ছেন। ম্যানহ্যাটানের ব্যস্ত বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে সেইসব শব্দসমষ্টি। কে জানে ভবিষ্যতের দরজায় গিয়ে পৌঁছবে কিনা।
আমার জীবনের একটি গভীর রোমাঞ্চের মুহূর্ত হয়ে রইল, এক অমূল্য ভালোবাসার বিকেল।