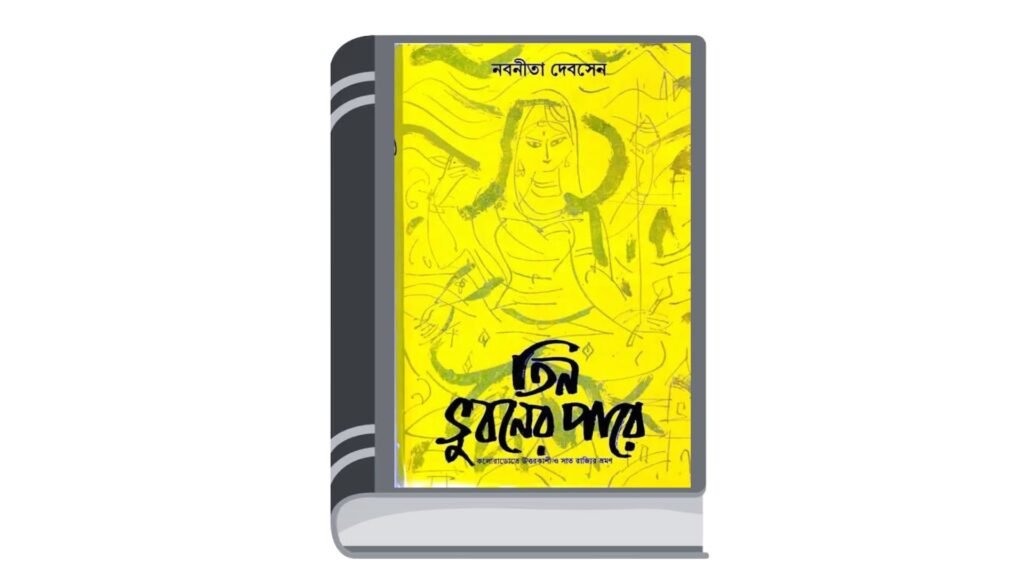পূর্ব জার্মানির চিঠি ১৯৭৯
অল্প অল্প বরফ পড়ছে এখনও-মেঘলা সকাল। ছোট শহরটার নুড়ি বাঁধানো রাস্তা দিয়ে মানুষজন হাঁটছে সবার গায়েই মোটা কোট, মাথায় টুপি, হাতে দস্তানা, পায়ে বুটজুতো—ডিসেম্বরের সকাল। ভাইমার শহরের আজ একটা শান্ত নিস্তব্ধ শোভাযাত্রা বরফ ঢাকা টাউন স্কোয়্যার পার হয়ে গেল। ক্রানাথ মিউজিয়ামের ওদিক দিয়ে এসে, মিছিল বেঁধে ভাইমার গির্জেয় প্রবেশ করছেন পূর্বজর্মনীর বহু গণ্যমান্য মানুষ। বিদ্বজ্জন, ধর্মযাজকেরা, সরকারি রাজপুরুষরা ছাড়াও শোভাযাত্রায় আছেন এই শহরের যত বিশিষ্ট নাগরিক। ক’দিনের তুষারপাতে প্রত্যেকটি বাড়ি শুভ্র : রাস্তাঘাট, গাছপালা, মাঠ-ময়দান সাদায় সাদা বর্ণহীন হয়ে আছে। আজ হেরডেরের ১৭৬তম মৃত্যু বার্ষিকী। এই হেরডেরকে সসম্মানে ভাইমার শহরের গির্জের অধ্যক্ষ করে নিয়ে এসেছিলেন স্বয়ং কবি গ্যয়টে। তাঁর মানুষ চেনায় ভুল হয়নি।
গির্জের এক কোণে শত জনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি একলা একটি মাত্র ভারতীয় ভক্ত। হাতে দুটি লাল গোলাপফুল। ছিল তিনটি। এইমাত্র একটি নামিয়ে রেখেছি হেরডেরের সমাধির ওপরে, অন্যদুটি গ্যয়টে আর শিলারের জন্য বুকের কাছে ধরা
এখনও, ঠিক যেন, বিশ্বাস হচ্ছে না আমি ভাইমারে। এই মাটি ভাইমারের মাটি। ওই বেদী থেকেই একদিন প্রার্থনা পরিচালনা করতেন স্বয়ং হেরডের, যাঁর কল্যাণে জার্মানিতে শেক্সপিয়ার এলেন অনুবাদের মাধ্যমে, এবং শুরু হল জার্মানির নবজীবন। কে জানত তাঁর নিজের গির্জেতে তাঁর ১৭৬তম মৃত্যু দিবসের প্রার্থনাসভায় তুমিও যোগ দেবে? জানাবে তোমারও কৃতজ্ঞতা? বিশ্বসাহিত্যের মঙ্গল সূচনায় হেরডেরের দান অনেক। সেই কল্যাণের সামগ্রিক ছত্রছায়ায় ঠাঁই পেয়েছে প্রত্যেকটি সাহিত্যপ্রিয় মানুষ। প্রার্থনা শেষে গির্জা থেকে বেরিয়ে খুব সাবধানে পা ফেলে হাঁটি। বরফে পথ পিছল, মাথায় কোটের হুডটা তুলে দিয়েছি, কান ঘেঁষে তুলে দিয়েছি কলার, হু হু করে ঠান্ডা বাতাস দিচ্ছে। গ্যয়টে পার্কের গাছগুলো অল্প অল্প দুলছে সেই বাতাসে ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ছে বরফ, প্রতিটি লতাগুল্ম পর্যাপ্ত তুষার স্তবকাবনম্র হয়ে আছে, যৌবনভারাবনমিতা গৌরীর শুভ্র লাজুক চেহারার নকল করছে বুঝি। গ্যয়টের বাগানবাড়ি, বিজন বিচ্ছিন্ন অট্টালিকাটি একটু উঁচু জমিতে দাঁড়িয়ে আছে। একক। ছায়াশূন্য নুড়ি বিছানো পথ। আজকের দিনে এ বাড়িটি দর্শকের জন্য খোলা নেই, অনেক আশা করে কাছে গিয়ে দরজা থেকে ফিরে আসি। দ্বার খোলা নেই। অগত্যা সরে যাই, আপন মনে হাঁটতে থাকি একা, সেতুটার ওপরে এসে এক মিনিট থমকে দাঁড়াই। নিচে দিয়ে ত্বরিৎ গতিতে বয়ে যাচ্ছে ইম্মনদী। হঠাৎ খেয়াল হয়, এমনিই কোনো তুষারঝরা ডিসেম্বরের সকালে গ্যয়টেও নিশ্চয় তাঁর বাগান বাড়ির দরজা খুলে হেঁটে এসেছিলেন নুড়ি বাঁধানো পথ দিয়ে। এই সেতুর কাছে–হয়তো এমনিভাবেই তিনিও কনুই ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিলেন এই কাঠের রেলিঙে, তাকিয়ে ছিলেন অন্যমনস্ক হয়ে নিচে বহমানা স্রোতস্বতী ইল্মের ছটফটে জলের দিকে। ঠিক এইখানে এই রেলিঙের ধারে। এমনিই বিষণ্ণ নির্জন সকালে।
বাগানটি দেখেই মনে পড়ে গেল, নতুনপন্থী গ্যয়টে ছিলেন ফরাসীবিমুখ, অ্যাংলোফিল। অষ্টাদশ শতকে জার্মানি এবং অস্ট্রিয়াতে সমস্ত ধনীর বাগানই ছিল ফরাসী কেতাদুরস্ত “ফর্মাল গার্ডেন।” অর্থৎ মাপা জোকা, হিসেব করা প্রতি সম-কোণের জ্যামিতিক অঙ্কে সুপরিকল্পিত। যেন মঞ্চে সাজানো নকল গাছ, পথ, ফোয়ারা। কোথাও কোনও বেনিয়ম নেই। ছক-কাটা, হিসেবি মনের পরিচয় তাতে। ভোর্সাই প্রাসাদের সেই বিখ্যাত বাগান, ভিয়েনার প্রত্যেকটি অপরূপ প্রাসাদোদ্যান, নয়াদিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনের মুঘল গার্ডেন্স, কাশ্মীরের নিশাতবাগ, এই পদ্ধতির বাগান। এর বিপরীত ধারার প্রচলন ছিল ইংল্যান্ডে—যার নাম “ল্যান্ডস্কেপ গার্ডেনিং।” জমির প্রাকৃতিক রূপকে যতটা সম্ভব অনাহত রেখে, নৈসর্গিক ছন্দের অনুকূলে স্বভাবসুন্দর বাগান সাজানো হত—সযত্নে “অযত্নলালিত” জংলী শোভা সৃষ্টির চেষ্টা থাকত তাতে, বাগানের মাঝখান দিয়ে নদীকে বয়ে যেতে দেওয়া হত, ঝর্ণাও তৈরি হত, গাছপালা পোঁতাই হত অজ্যামিতিক উপায়ে। এ বাগানও তাই। মনে হতেই একটা শিহরণ বয়ে যায় শিরদাঁড়া দিয়ে। এই পার্কেই একদিন গ্যয়টে শার্লট ফন স্টাইনের সঙ্গে গলাগলি করে হেঁটে বেড়িয়েছেন। এমনি পাতাঝরা গাছের ফাঁক দিয়ে হয়তো জ্যোৎস্না এসে পড়েছে তাঁদের ওপরে, কবোষ্ণ চাঁদের আলোয় নির্জন বরফ আহ্লাদে গলে যেতে চেয়েছে। এখন শীতকাল, এটা বাগানে বেড়ানোর সময় না। কিন্তু রুশো যেমন বলেছিলেন, “শীতকালেই বরং আমার বসন্তের বর্ণনা করতে ভাল লাগে”—তেমনি এই তুষার ঢাকা পার্কে দাঁড়িয়েই আমিও দিব্যি দেখতে পেলাম বসন্ত মঞ্জরিত শ্যাম শোভন একটি জীবন্ত বাগান। দীর্ঘ সুঠাম এক কবির পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছেন সোনালি চুলের নরম একটি যুবতী, ঝাঁকড়া সবুজ পাতা থেকে তাঁর চুলে ঠিকরে পড়েছে বাসন্তী সূর্যের আলো।
একটু আগেই লটের প্রাসাদোপম বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলুম, তখন মনে হচ্ছিল এক্ষুনি বুঝি একটা জমজমাট জুড়ি গাড়ি এসে থাকবে, লাফিয়ে নামবেন যুবক গায়টে অধৈর্য হয়ে নাড়বেন ওই কারুকার্য করা বিশাল ভারী দরজার মস্ত লোহার কড়া—ঘরের মধ্যে প্রতীক্ষা করে আছেন সুন্দরী লটে—। আকৈশোর যাঁদের কথা কেবল বইতেই পড়েছি, আজ সশরীরে দাঁড়িয়ে রয়েছি তাঁদেরই দেশ ছুঁয়ে। যেন স্বপ্নের রাজ্যে এসে পড়েছি, এত সৌভাগ্য যেন সত্য নয়। এ আমার পাবার কথা নয়।
খোয়া বাঁধানো রাস্তার প্রত্যেকটা মোলায়েম কালো নুড়ি, ঠান্ডা বাতাসে উড়ে পড়া প্রত্যেকটা শুকনো পাতা ভাইমারের বিষয়ে একটা না একটা গোপন কথা উচ্চারণ করবে তোমার কানে। গ্যয়টের নামের মন্ত্র দিয়ে তোমার চারদিকে গড়ে তুলবে একটা ম্যাজিক বেড়াজাল।
ছোট্ট তিনতলা হলদে বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে দেখলুম ঝুলছে—”আজকের মতো জনসাধারণের জন্য বন্ধ।” হা কপাল আমার। বন্ধ? শিলারের দরজা আমাদের কাছে বন্ধ থাকা উচিত? হঠাৎ অভিমান হয়ে যায়—জনসাধারণ? কে জনসাধারণ? আমরা তো একই পরিবারের মানুষ। হতে পারি নগণ্য, অতি তুচ্ছ, গরীব আত্মীয়। গ্যয়টে শিলারের মতো হীরের ঝলক নেই নামের গায়ে, কিন্তু রক্তে আছে তো গভীর যোগাযোগ। আছে গোপন আত্মীয়তার চিহ্ন। জগতের লেখকজাতি না একই পরিবার? ‘ভেল্ট লিটেরাট্যুর’ বিশ্বসাহিত্যে এই শব্দ তো এই ভাইমারেই উচ্চারিত হয়েছে। দূরের, কাছের, যুবক, বৃদ্ধ, নামী, অনামী, জীবিত, মৃত, অমর—যারাই লিখি, সবাই না একসূত্রে গাঁথা একটি অচ্ছেদসহন পরিবার? হায়, শিলার তো জানলেন না, তাঁর এক নিকট আত্মীয় বহুদূর থেকে এসে দরজায় কড়া নেড়ে ফিরে যাচ্ছে।
এমন সময়ে পাশেই কেউ কথা বলে ওঠে। তিনতলার একটি খোলা জানালার দিকে আঙুল তুলে ধরেছে একটি যুবক। পথের ধারে বেঞ্চিতে বসে আছে সে। “ওই যে, ঐ জানালাটার দিকে তাকাও, ওই যেখানে টাটকা ফুলের গোছা রয়েছে ওইটেই শিলারের শোবার ঘর। ওই ঘরেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।”
ইংরিজিতে কথা শুনে আমি তো তাজ্জব। কেননা এ তো ভাইমার, পূর্ব জার্মানি। পশ্চিম জার্মানির মতো এখানে মোটেই ইংরিজির ছড়াছড়ি নেই। এ যে ভিন্ন রাজত্ব। ওখানে পথে ঘাটে মার্কিন সৈন্যদের ফুর্তির হুল্লোড়। পশ্চিম বার্লিনের রাজপথে একটি মাত্র মার্ক দিলেই দেখা যায় “সেক্স-পিপ-শো”, জানলার ফুটোয় চোখ রেখে দাঁড়াও, ছোটবেলার সেই ‘দিল্লিকা কুতব দেখো, আগ্রাকা তাজ দেখো, বুম্বই কা গেট দেখো’-র মতন দাঁড়ালে, দেখা যায় ঘুমন্ত, গোলাপী ভেলভেটের রিভলভিং বিছানায় জীবন্ত নগ্ন যুবতী মেয়ে আলিস্যিতে আড়মোড়া ভাঙছে। মাত্র এক মিনিট। তারপরেই ঘণ্টা বেজে উঠবে। আমার ভীষণ মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। খুবই ব্যাজার মুখে, বছর ষোলো-সতেরোর একটি পরমা সুন্দরী মেয়েকে ওই ভাবে ওই কাজে নিযুক্ত দেখে। সঙ্গের বন্ধুরা তাড়াতাড়ি বললেন—”এ মেয়েরা কিন্তু দেহ ব্যবসায়ী নয়, ঘণ্টা হিসেবে কাজ করে চলে যায়, বাণিজ্য মাত্র। শিল্পীর মডেলের মতো, নগ্ন দেহ দূর থেকে প্রদর্শন করে, ওরা অর্থোপার্জন করে। বেশির ভাগই কলেজের ছাত্রী।” অবাক হয়ে ভাবি এরাই আবার উইমেন্স লিব নিয়ে বিক্ষোভ করে। মন খারাপ হল এই ভেবে, এতদিন ধরে এখানে সৈন্যের বসবাস না হলে শহরটার নৈতিক মান হয়তো এমনধারা উচ্ছন্নে যেত না। এ তো স্পষ্টই ঘরছাড়া, ব্যারাকবাসী, বুভুক্ষু পুরুষের দৃষ্টিক্ষুধা মেটানো। অর্থোপার্জনের কি অন্য পথ এদের নেই?
পূর্ব জার্মানিতে ব্যাপারটা অন্য রকম। নৈতিক আবহাওয়া একেবারেই বিপরীত। নগ্নতা তো দূরের কথা কোথাও সিনেমার বিজ্ঞাপন পর্যন্ত চোখে পড়বে না। এমন কি পূর্ব বার্লিনেও চোখে পড়বে না নাইটক্লাব, কি ক্যাবারে। কেবল দেখছি এই শান্ত মফঃস্বল শহরেরও নুড়ি বাঁধানো বুক কাঁপিয়ে মাঝে মাঝেই কুচকাওয়াজ করে যাচ্ছে দেশীবিদেশী তরুণের দল, তাঁদের কাঁধে ভারী বন্দুক, পরনে ভারী ইউনিফর্ম, পায়ে ভারী বুট, মুখগুলিতে গোঁফদাড়িও ওঠেনি এখনও চলেছে তরুণ রুশ সৈন্যদের নগর প্রহরা। ভাইমারের মতো শহরে দৃশ্যটা বড়ই বেমানান জানিনা কোনটা বেশি অশ্লীল। তরুণীর নগ্ন যৌবনের, না সৈন্যদের নগ্ন শক্তির প্রদর্শনী। এত বছর ধরে জার্মানির বুক চিরে ফেলে, বসেই রয়েছে দুই পরদেশী সৈন্যের দল। ওপারে তুমি রাধে এপারে আমি। ব্যবস্থাটার অস্বাভাবিকতাটা আর চোখেও পড়ে না আমাদের। জীবন এতই দূরে সরে গিয়েছে স্বাভাবিকতা থেকে।
শিলারের বাড়িতে ঢুকতে না পারি তাঁর ঘরটা দেখতে পেলুম, জানলায় একগুচ্ছ রঙিন ফুলের ঝলক দেখতে পেলুম, তাতেই ধন্য, তাতেই আমি খুশি। ওই জানালায় দাঁড়িয়ে কবি শিলার নিশ্চয়ই কতবার এই রাস্তার দিকে তাকিয়েছেন—আমি যেখানটায় দাঁড়িয়ে রয়েছি, ঠিক সেখানটাতেও তাঁর দৃষ্টি নিশ্চয় বহুবার ঘুরে গেছে। কোনও দিন কি তিনি ভাবতে পেরেছিলেন যে তাঁর মৃত্যুর দেড়শো বছর পরে সুদূর ভারতবর্ষ থেকে একটি বাঙালি মেয়ে তাঁর জন্য গোলাপ ফুল হাতে করে এই জানালার নিচে এসে দাঁড়াবে? এক মহৎ কবির কাছে এক তুচ্ছ কবির অর্ঘ্য নিয়ে?
এই পথ একদিকে চলে গেছে জার্মানির জাতীয় নাট্যশালার দিকে, অন্যমুখে হাঁটলে পাওয়া যাবে গ্যয়টের বসতবাড়ি। আমি চলতে থাকি, ভাইমারের জর্মন ন্যাশানাল থিয়েটারের দিকে। এই সেই প্রতিষ্ঠান, গ্যয়টের সার্থক স্বপ্ন—চল্লিশ বছরেরও বেশি দিন ধরে পরিশ্রম করে নিজের হাতে এটিকে তিনি গড়ে তুলেছিলেন। আর সেই কর্মযজ্ঞে শিলার ছিলেন তাঁর বিশ্বস্ত সহকারী। জার্মান জাতীয় নাট্যশালার সামনেই এক মহান দৃশ্য! খুব উঁচু বেদীর ওপরে দুটি প্রাণোচ্ছল তেজস্বী মানুষের যুগ্মমূর্তি। একটি তরুণ আর এক প্রৌঢ়, হাত ধরাধরি করে এগিয়ে যাচ্ছেন। দূর ভবিষ্যৎকালের দিকে তাঁদের স্বপ্নময় দৃষ্টি, তাঁদের দৃঢ় পদক্ষেপণ। যেন কালজয়ী শিল্পী হৃদয়ের মূর্তরূপ—। গ্যয়টে আর তাঁর তরুণ বন্ধু শিলারের এই যুগল প্রয়াসের ফলে জার্মানির কত দূর সাংস্কৃতিক অগ্রগতি হয়েছিল, তা ইতিহাস আমাদের বলেছে।
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বোমা পড়ে বেশ বড় রকমের ক্ষতি হয়েছিল জাতীয় নাট্যশালার। আবার অতিযত্নে তার পুননির্মাণ করেছেন বর্তমান সরকার। সেখানেই চলেছে হেরডের সেমিনার উপলক্ষে সাংস্কৃতিক উৎসব। বিকেলে ওখানে বেঠোফেন উৎসবে আমারও নেমন্তন্ন।
পূর্ব জার্মানিতে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি পূরণের এই প্রচেষ্টাটি কিন্তু সত্যি দেখবার মতো। বড় বড় প্রাসাদগুলিকে ঠিক অবিকল আগের মতো করে গড়া হচ্ছে। ভাস্কর, শিল্পজ্ঞ, বিজ্ঞানী, স্থপতি, ঐতিহাসিক, সকলকে নিয়ে পরামর্শ করে কমিটি গড়ে সরকার এই পুনর্গঠনের কাজগুলি করছেন। পূর্ব-বার্লিনের একদা বিধ্বস্ত লিনডেন অ্যাভিন্যুতে দেখেছি রাজপথের দুধারে আবার লাগান হয়েছে লিডেন তরু, প্রাসাদোপম অট্টালিকাগুলিও প্রায় সব সম্পূর্ণ।
‘ভাইমার’ বললেই মনে আসে ‘গ্যয়টে’ এই অদ্বিতীয় নাম। অথচ, যুক্তিযুক্ত হত আরও অনেক নামের ভিড় জমে ওঠা, মনের মধ্যে। ভাইমার নামের সঙ্গে য়ে সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গের জ্যোতির্বলয় জড়ানো আছে, তাতে বিভিন্ন প্রতিভার রশ্মি মিলেছে এসে। যেমন ভীলান্ড আর হেরডের, যেমন বাখ, ভাগনার আর লিস্ট, যেমন লুকাচ ক্রানাখ, যেমন ফ্রেডেরিক দ্য গ্রেট এবং ভোলত্যার, যেমন কার্ল আউগুস্ট এবং গ্যয়টে আর শিলার। এঁরা প্রত্যেকেই ভাইমার নামটিকে রূপকথায় পরিণত করতে সহায়তা করেছেন। কিন্তু এগুলি ঐতিহাসিক তথ্য মাত্র, হৃদয়সত্য হয়ে ওঠেনি। আগেই গায়টে এই নাম অজস্র স্মৃতির স্মৃতিকণায় মেঘ উড়িয়ে অন্য সব নামগুলি আচ্ছন্ন করে ছুটে আসে। ‘হবাইমার’ আর ‘গ্যয়টে’ আজ অচ্ছেদ্য।
সকলেই জানি যে, একজন লেখকের পরিচয় তাঁর লেখায়। পরিচিত হবার জন্য তাঁর বাসগৃহ ধাওয়া করবার কোনও প্রয়োজন নেই। কে না জানে মক্কায় না গেলেও খাঁটি মুসলমান হওয়া যায়, যীশুকে চেনবার জন্য জেরুজালেম যাবার দরকার নেই। তবুও জেরুজালেম জেরুজালেমই, মক্কা মক্কাই। যেমন শান্তিনিকেতন গেলে রবীন্দ্রনাথের, তেমনি য়াসনাইয়া পলিয়ানাতে গেলে টলস্টয়ের, আর ভাইমারে গেলে গ্যয়টের আরেকটু কাছাকাছি হওয়া যায়। কোনো লেখকের ব্যক্তিগত জীবনী যে কারণে আমরা পড়ি, বা তাঁর ছবি যে কারণে দেখি, বাড়িও সেই কারণেই একটা পরিচয় দেয়। মানুষটার সঙ্গে দেখা হয়, শিল্পীর বাইরেও যে-মানুষের অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব। অনেকটা চিঠিপত্র যেমন, তেমনিই মানুষের বসতবাড়ি। সেখানে তার রুচির একটা ছাপ পড়ে আর মূল্যবোধেরও।
অবশ্য সব বাড়ির ক্ষেত্রে একথা হয়তো খাটবে না। কোথাও গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। আবার কোথাও চিরাচরিত প্রথাই সব। শেক্সপিয়ারের বাড়িতে, কিংবা অ্যান হ্যাথাওয়ের কুটিরে শেক্সপিয়ারের প্রতিভার কোনও অনন্য ছাপ কিন্তু নেই। ঐ বাড়িগুলি ষোলো শতাব্দীর স্ট্র্যাটফোরডের যে কোনো ভদ্র মধ্যবিত্তেরই গৃহ হতে পারত। যেমন “ডাভ্ কটেজ” এ আমি ওয়ার্ডসওয়ার্থের তেমন কোনও বর্ণগন্ধ পাইনি। কিন্তু “উত্তরায়ণ” বাড়ি তা নয়। সেখানে এক বিশিষ্ট প্রতিভার শিল্পরুচির ছাপ আছে। গ্যয়টের প্রাসাদও অনন্য। ধরা যাক যদি আমি টিকিট না কাটতুম—যদি পথে হাঁটতে হাঁটতে আপনিই ঢুকে পড়তুম বাড়িটাতে এক গেলাস জল চেয়ে নেব বলে,—তাহলে ঢুকেই তো শ্বাস রুদ্ধ হয়ে যেত—প্রকাণ্ড জুনোর মুখ দেখে।—”বাপ্ রে। এ বাড়ি কার? কোন্ গৃহস্বামীর?”
দুই
বাইরে থেকেই হলুদ বাড়িটা বড়, কিন্তু ভিতরে ঢুকলে যেন আরও বড়। বিশাল, মহিমাময় অসামান্য সব শিল্পকর্মে কানায় কানায় ভরা। প্রথমে মনে হবে বুঝি কোনও জাদুঘরে ঢুকে পড়েছি। কিন্তু যদি জানি যে এটা সাধারণ জাদুঘর নয়, একজনের ব্যক্তিগত বাসগৃহ, তবে ওটা যে একমাত্র য়োহান ভোলফগাং ফন গ্যয়টের না হয়ে যায় না, সে কথা তাঁর কোনো পাঠককেই বলে দিতে হবে না।
বাড়িটা সত্যিই একটি আশ্চর্য মানুষের জীবনচর্যার সাক্ষ্য। তাঁর স্মৃতি-সত্তা-স্বপ্নকে বুকে ধরে রেখেছে। যেন তার মালিকের বিপুল বিচিত্র ব্যক্তিত্বের একটা বহুমাত্রিক ছবি এই গৃহ। স্বদেশেও রুচিমান ধনীব্যক্তির শিল্পসংগ্রহ দেখার ভাগ্য হয়েছে, হায়দ্রাবাদে সালার জং সায়েবের অসামান্য ব্যক্তিগত শিল্প সংগ্রহের কথা সবাই জানি, কলকাতার মল্লিকবাড়ি নিয়ে যথেষ্ট গৌরব করতে পারি আমরা। কিন্তু গ্যয়টে-গৃহ একটু আলাদা ব্যাপার।
শুধু শিল্পবোধ নয়, এখানে আছে পরিব্যাপ্ত, পরিমার্জিত, জ্ঞানতৃষ্ণার সঙ্গে জীবনের প্রতি সীমাহীন ভালবাসা। একটি ব্যক্তিত্বের পূর্ণ স্বাক্ষর। কার বাড়ি না-জানলেও ক্ষতি নেই, ঘর থেকে ঘরে হেঁটে যেতে যেতে আপনিই উত্তর জানা হয়ে যাবে।
শহরের নাম যখন ভাইমার। এমন বাড়ি সুদূর ইতালিতে হয়তো আর একটি মাত্র মানুষেরই থাকতে পারত, আরও দুশ বছর তাঁর বয়স বেশি, তাঁর নাম লিওনার্দো দা ভিনচি। কিন্তু তাঁর না ছিল সংসারে সে সঙ্গতি, না চিত্তের সে স্থিরতা। এ বাড়ির প্রতিটি কামরাই স্বতন্ত্র চরিত্রে উদ্ভাসিত। এক একটি ঘর যেন মানুষ গ্যয়টের অন্তর্লোকের এক একটি বিচিত্র মহল।
অথচ বিস্ময়ের কিছুই ছিল না। সত্য বলতে কি তেমন খবর একটিও কুড়িয়ে আনিনি ও বাড়ির মেঝে থেকে, যা কলকাতায় বসে বই পড়ে জানা যায় নি। কিন্তু সেই জানা, আর এই জানা? একটা ছিল মননগ্রাহ্য—তত্ত্বমাত্র। অন্যটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। প্রত্যক্ষ অনুভব। আসমান জমিন ফারাক। পৃথিবীতে সমুদ্র আছে, তাতে অনন্ত তরঙ্গ আছে, সবাই জানি। কিন্তু সে-জানার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সমুদ্র দর্শন, স্নানের মধ্য দিয়ে লবণাক্ত সিন্ধুকে জানা কি এক? এও তেমনি। ভাইমারে না এলে আমার এমন করে স্নায়ুতে-মজ্জায় জানা হত না গ্যয়টে কেমন মানুষ। জ্ঞাত তথ্য বটে, তবু যখন দেখি পরপর চোদ্দ পনেরোটা বিপুল দেরাজ ভর্তি বিশাল বিশাল মানচিত্র গোটানো রয়েছে, টেবিলের উপরে সযত্নে রাখা গ্লোবটি, তখন টের পাই গ্যয়টের ভূগোলপ্রীতি কী বস্তু। ভূগোল থেকে ভূতত্ত্বে হাজারটা বড় পাথর, স্ফটিক, প্রবাল, ফসিল, স্ট্যালাকটাইট, নদীর নুড়ি, ধাতু ভরা খনিজ পাথর, রত্ন—কী নেই? বিশেষভাবে তৈরি বাক্সে সাজানো আছে সব। যত্নে লেবেল দেওয়া রয়েছে। লেন্সের নিচে এখনও স্লাইড আঁটা, যেন এক মিনিটের জন্য তিনি একটু ও ঘরে গেছেন। সৃষ্টির রহস্য উন্মোচনের জন্য কী তীব্র আকুলতা। প্রত্যেকটি কামরা যেন আমাদের ডেকে ডেকে বলে–দ্যাখো, চেয়ে দ্যাখো বিশ্ব-প্রকৃতির প্রতি কী অধীর আগ্রহ এই মানুষটির, প্রেমিকের যেমন থাকে তার প্রেমিকার প্রতি। তেমনিই নিরাবরণ করে, তন্ন তন্ন খুঁজে উলটে পালটে প্রকৃতিকে চিনে নিতে চাইছেন একজন, দূরের নক্ষত্রটিকেও হস্তগত আমলকী করে ফেলতে যাঁর দুর্দম স্পৃহা।
একটা কাচের বাক্স ভর্তি কেবল প্রজাপতি। হাজার রঙের খেলা এখনও দুশো বছর বাদেও অম্লান রয়েছে তাদের উড়ালহারা পাখনায়। গ্যয়টের আঙুলগুলি কত সাবধানে সঞ্চারিত হয়েছে, যাতে ওই সুকুমার বর্ণ রেণু মুছে না যায়, ঝরে না পড়ে। মানুষটির মমতার ছোঁয়া লেগে রয়েছে প্রত্যেকটা রঙের ফোঁটায়।
আর একটি ঘর ভর্তি কেবল ছোট বড় পাখির কঙ্কাল, সাবধানে মাউন্ট করা, কবির জীববিদ্যার উৎসাহের প্রমাণস্বরূপ দাঁড়িয়ে। অন্য এক জায়গায় টেবিল ভর্তি কাচের নীচে সাজানো নানান দেশের মুদ্রার সংগ্রহ।
কামরার পর কামরা, বারান্দার পর বারান্দা উপছে পড়ছে ছবিতে আর মূর্তিতে।
দরজার দুপাশে শিলারের আর হেরডেরের আবক্ষ মর্মরমূর্তি সাজানো। এখানেই শিলারের সামনে রেখে দিলুম তাঁর নাম করে বয়ে আনা লাল গোলাপটি।
যে সুবৃহৎ জুনোর মুখটি আমাদের গ্যয়টের গৃহে অভ্যর্থনা জানাল, তার ফোটো অনেক দেখেছি, কিন্তু চোখে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। এত বিশাল! এত বড় জিনিসটি উনি ইতালি থেকে বয়ে এনেছিলেন?
ইতালিযাত্রা তাঁর জীবনকে পালটে দিয়েছিল। একদিকে থেকে তাঁকে করে তুলেছিল ঐশ্বর্যবান অন্যদিকে দরিদ্র। শার্লট ফন্ স্টাইনের সঙ্গে দুলর্ভ অমূল্য মানবিক সম্পর্কটি ছিন্ন হয়ে গেল ঐ দূরত্বকালে।
ক্রিস্টিনার নামে একটি ঘর আছে, অনেকগুলি ছবি দেখলাম তাঁর। একটি ঘুমন্ত ক্রিস্টিনার স্কেচ, গ্যয়টের নিজের হাতে আঁকা, কোঁকড়াচুলে ঘেরা সরল মিষ্টি কচি মুখটা দেখলেই মায়া হয়। হয়তো খানিকটা বোঝাও যায় গ্যয়টে কেন এই সবদিক থেকেই অসম, ঘরকন্নার কাজের জন্য নিযুক্ত দরিদ্র মেয়েটিকে শেষ পর্যন্ত বিয়েই করে ফেলেছিলেন। শোনা যায় ক্রিস্টিনা ছিলেন খুব প্রাণোজ্জ্বল, প্রকৃতির খুবই কাছাকাছি ছিল তাঁর স্বভাবসুন্দর অস্তিত্ব। কবির শরীরে মনে তিনি নিশ্চয় একটা অনন্য সবুজ স্বাদের ছুটির বাজনা বাজিয়ে দিতেন। তাঁকে লেখা অনেকগুলি চিঠিও এখানে রয়েছে গ্যয়টের। ক্রিস্টিনা ও গ্যয়টের পুত্র সন্তানটিরও একটি সুন্দর স্কেচ দেখলুম, কবির নিজের হাতে আঁকা। আছে শার্লট ফন্ স্টাইনের ছবিও।
কোনওদিন কি স্বপ্নেও ভেবেছিলুম যে গায়টের বাড়ির দেওয়ালে টাঙানো শার্লটের ছবির দিকে স্বচক্ষে চেয়ে থাকব? এই আমি? এসব মুহূর্তে বন্ধুদের জন্য মন কেমন করে। যখনই ভাল কিছু দেখি, যখন মনটা ভরে ওঠে, পরমুহূর্তেই মনে হয়, আহা, এটা আমিই মাত্র একা দেখছি—ওদের এনে দেখাতে পারলে আরও ভাল লাগত।
দেখতে-দেখতে, মুগ্ধ মোহিত হতে হতে একটা জিনিস খেয়াল হল। এত যে গ্যয়টের ভারত চর্চার কথা শুনি, তাঁর স্বহস্তে পোঁতা একটি গাছও দেখলাম ভাইমারে এসে যার প্রতিটি পাতা দ্বিমুখী—গ্যয়টে বলতেন তার জীবনদর্শনের প্রতিবিম্ব ওই পাতাগুলি—পূর্ব পশ্চিম দুই দর্শনের ডগাদুটিই বিভক্ত, কিন্তু বৃত্তে তারা অভিন্ন। মূলের জীবনরসেও তারা একই অমৃত পান করছে। কিন্তু তাঁর অগুনতি শিল্প সংগ্রহের মধ্যে ভারতীয় শিল্পের একটিও নমুনা দেখিনি। নমুনা দেখিনি চীনে জাপানী ছবিরও।
বিশাল গ্রন্থাগার। প্রচুর বই, বেশ কয়েক হাজার। শেক্সপীয়রের সঙ্গে আছেন কালিদাস আর হাফিজ, সেই বিশ্ববিখ্যাত অভিজ্ঞান শকুন্তলম, আছেন বাইরন আর কারলাইল, রুশো আর পুশকিনের পাশাপাশি। কালিদাস ভিন্ন আর কিন্তু কোনো ভারতীয় সাহিত্য চোখে পড়ল না। গ্যয়টে গৃহের বিপুল বিস্তার সংস্কৃতিচর্চার মধ্যে ভারতবর্ষের স্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হল না। তাঁর বহু-আলোচিত ভারত প্রেমের কোনও সাক্ষাৎ প্রমাণ নজরে এল না। যদিও তাঁর বিভিন্ন রচনায়, চিঠিপত্রে, আত্মজীবনীতে তার টুকরো টুকরো বহু প্রমাণ ছড়ানো। এমনকী তিনি যে দেবনাগরী হরফ লিখতে শিখছিলেন,—তারও ফোটোস্ট্যাট প্রতিলিপি আমরা দেখেছি দেশে, যেমন আরবী হরফও লিখতে শিখেছিলেন। হিন্দু দেবদেবীদের পৌরাণিক গল্পে, মিথলজিতে গ্যয়টের উৎসাহ নানা ভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। গ্যয়টের সমকালেই, জার্মানিতে সংস্কৃতচর্চার বান ডেকেছিল। ইংল্যান্ডে সদ্য আবিষ্কৃত হয়েছে এই নবদিগন্ত,—জার্মানিও প্রায় ইংলন্ডের সঙ্গে সঙ্গেই সেই দিগন্তের হদিশ পেয়েছে হেরডের মারফৎ। শ্লেগেলভ্রাতারা সংস্কৃত নিয়ে মেতে উঠেছেন, হেগেল লিখে ফেলেছেন তাঁর ভগবদ্গীতার সমালোচনা। হয়তো লাইব্রেরির হাজার হাজার বইয়ের মধ্যে এসবও আছে। আমার ঝাঁকিদর্শনে নজরে আসেনি। গ্যয়টে-গ্রন্থাগারের পুস্তক-তালিকার একটা কপি সংগ্রহ করতে পারলুম না, তাই অনেক কৌতূহলের নিবৃত্তি হল না। ইচ্ছে ছিল দেখব ওলন্দাজ জাপারের ভ্রমণবৃত্তান্তটি, ফরাসি সোনরা’র সেই ছবিওয়ালা ভারততথ্য—শুনেছি গ্যয়টের ভারতচর্চার উৎসাহ যুগিয়েছিল কালিদাস ছাড়াও, এইসব বইয়ের গল্প।
যদিও প্রাচ্যের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর যথেষ্ট কৌতূহল এবং সম্ভ্রমবোধ ছিল, শেষ পর্যন্ত কিন্তু প্রাচ্যের শিল্পে, ধর্মে, বা দর্শনে গ্যয়টের আন্তরিক রুচি ছিল বলে মনে হয় না। একেরমান ও বলেছেন যে গ্যয়টে ভারতীয় দর্শনে উৎসাহী ছিলেন না। তিনি মনেপ্রাণে ক্রিশ্চান, তাঁর সম্পূর্ণ জীবনদর্শন একান্ত ভাবেই শুদ্ধ খৃস্ট্রীয় মতাবলম্বী। গ্যয়টে গৃহের চরিত্র দেখেও এই কথাই মনে হল। ‘বিশ্ব’ তাঁর স্বপ্ন হলেও ইওরোপই তাঁর সত্য, হৃদয়, মনীষা; মনসা যে-সত্যকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।
এহেন সর্বশিল্পসাধক বাড়িতে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের একটি সংগ্রহ থাকা স্বাভাবিক ছিল। হয়তো অন্যত্র আছে, জানি না। সবই কি দেখেছি? কি জানি? হয়তো কিছু বাকি থেকে গেল। কিছু বাকি রইল ভাবতেও আমার কেন জানি না, বেশি ভাল লাগে। থাকুক কিছু অনধিগত, থাকুক কিছু আড়ালে।
কখন পায়ে পায়ে এসে দাঁড়িয়েছি এই এক চিলতে ঘরটার দোর গোড়ায়। ছোট্ট সরু এক ফালি ঘর, এই জাঁকজমকালো প্রাসাদের বৃহৎ আড়ম্বরের সঙ্গে ঠিক মানানসই নয় যেন। বড্ড সাদামাটা অতিরিক্ত ছোট্ট। মাত্র একটিই জানলা বাগানের দিকে খোলে। কে থাকত এমন বাড়িতে, এই ঘরে? একটি ডেসক একটা তাপ মাপার জন্য একটা থার্মোমিটার আর আর্দ্রতা মাপার জন্য একটা হাইগ্রোমিটার, একটুকরো গাঢ় নীল (ল্যাপিস লাজুলি?) পাথর। কবিহৃদয়ের প্রতীকের মতো। অনাড়ম্বর একক শয্যাটি পাতা, পায়ের কাছে একটুকরো পশমের শতরঞ্চি, শীতের দিনে বরফ ঠান্ডা মেঝেয় যাতে পা নামাতে না হয়।
এই সজ্জাহীন, নিরলঙ্কার ঘরটিই ছিল ভাইমারের প্রধানমন্ত্রীর প্রতি রাত্রের আশ্রয়। এই বিপুল ঐশ্বর্যের যিনি মালিক তাঁর বিশ্রামক্ষেত্র। এই কি প্রধানমন্ত্রীর যোগ্য শয়নকক্ষ? আঠারো উনিশ শতকের ধনীদের শোবার ঘরে বিপুলায়তন চার-স্তম্ভের পালঙ্কগুলি কি দেখিনি অন্যত্র? মখমল, কিংখাব, সাটিন, লেসের ছড়াছড়ি—স্তরে স্তরে ঝালর, পর্দা, সেসব খাটের কাঠেই বা কত কারুকাজ। বারোক্ ধাঁচের মালা-পরী-দেবশিশু চর্চিত। আঙুরগুচ্ছ খচিত। কিন্তু এই শয্যা সম্পূর্ণ আলাদা। বিলাসবর্জিত। এ ঘর প্রায় তপঃক্লিষ্ট সন্ন্যাসীর ঘর। শয্যাটিতে নেহাৎ সাধারণ একটি রেশমী লেপ ঢাকা দেওয়া। প্রাসাদের চিরাচরিত মালিকরা সাধারণত এমনিতর কুঠুরিতে অধস্তন কর্মচারীদেরই মাথা গোঁজবার ব্যবস্থা করে দেন। কিন্তু এও তো কবির বাড়ি এও তো “আত্মানুশীলনেরই অন্য একটা দিক। যেমন আশ্চর্য তাঁর লেখবার আসন, ডেস্কের সামনে ঘোড়ার জিন লাগান টুলটা—যার দু পাশে পা ঝুলিয়ে বসে পিঠে হেলান না দিয়ে, গ্যয়টে লিখতেন—অশ্বারোহণের ভঙ্গিতে। তার মধ্যে যে কঠোর অনুশীলনের ইঙ্গিত আছে, এখানেও তাই। প্রত্যেকটি খাওয়া দাওয়াতেও গ্যয়টে ছিলেন অত্যন্ত সাদাসিধে। ব্যক্তিগত অভ্যাসের ক্ষেত্রে এই কঠোর অনাড়ম্বর রুচি অন্তঃপ্রকৃতির শুদ্ধাচারী সংযমের দিকটাকে আলোকিত করে। শিল্পের পক্ষে যা অপরিহার্য। শিল্পী তো অন্তরে সন্ন্যাসীই। বিলাসবিহীন, নিরাভরণ, রিক্ত এই কুঠুরিতে বহির্বিশ্ব থেকে পালিয়ে এসে দিন শেষে নিজের সঙ্গে কবির মুখোমুখি হওয়া। কর্মবহুল জনমুখর দিন কাটতো রাজসভায় বহুমুখী দায়িত্বের—রাত্রিবেলা আশ্রয় নিতেন বাগান ঘেঁষা একতলার এক ছোট একফোঁটা ঘরে, যেখানে তিনি নির্জন, অন্তর্মুখী, ঈশ্বরমুখীও। বয়োবৃদ্ধ মহাকবির শাস্ত মৃত্যু হয়েছিল এই ঘরে, এই শয্যায়, আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে, ১৮৩২ এর ২২শে মার্চ। চৈত্রের প্রথম। ভাইমারের বাতাসে তখন নবীন বসন্ত। জানলার বাইরের ওই ফুলবাগানে বরফ ফাটিয়ে জেগে উঠছে নীল হলুদ ক্রোকাসের কুঁড়ি।
এ ঘরের জানলায় কোনও ফুলদানি নেই। নেই মূর্তি, কি ছবির উপদ্রব। হলঘরগুলিতে যদি থাকে বিশ্বসংস্কৃতির ধারক-বাহকের দর্পিত মূর্তি, এ কামরার শূন্যতায় নম্রতায় ফুটে আছে এক চির-একাকী কবির ধ্যানমগ্ন রূপ। নিরহংকার অথচ উচ্চভিলাষী, আত্মস্থ অথচ দুঃখী। স্তব্ধ নৈঃশব্দ্যে যেন থমকে আছে গ্যয়টের শেষ নিঃশ্বাসের উষ্ণতা।
হাতে-ধরা শেষ গোলাপটি নত হয়ে এই চৌকাঠে স্থাপন করে, স্থির হয়ে দাঁড়ালুম।