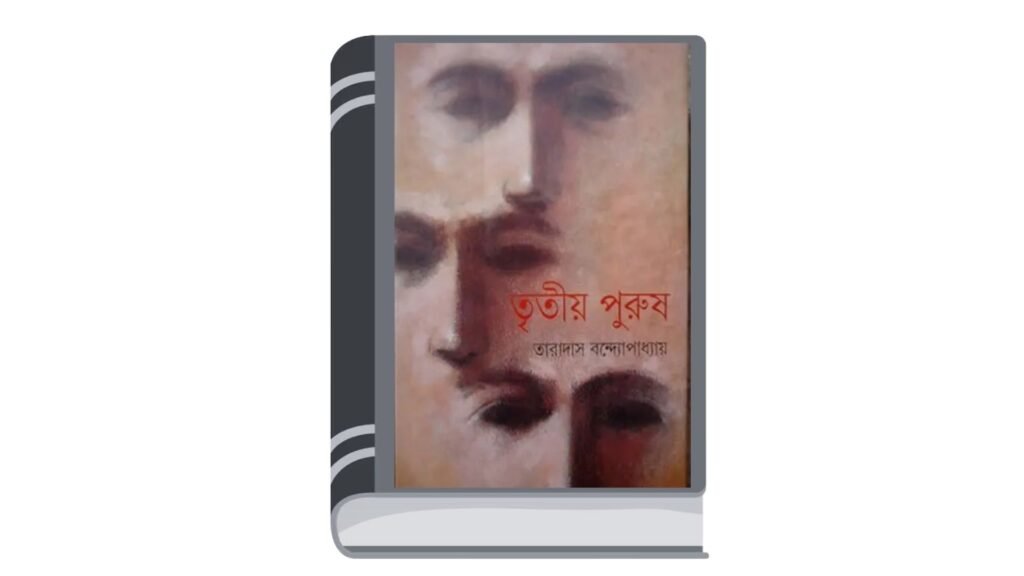২০. অল্পবয়েসে জীবনটা একরকম বেশ সুখে
বিংশ পরিচ্ছেদ
অল্পবয়েসে জীবনটা একরকম বেশ সুখেই চলিতে থাকে। মাথার ওপরে একটা বড়োসড়ো আকাশ, দিগন্ত অবধি বিস্তৃত পৃথিবী তার সমস্ত আনন্দ দুঃখ হর্ষ আর পথের প্রতি বাঁকে আস্বাদিত চমক লইয়া অপেক্ষা করিয়া আছে। সবকিছুই ঘটতে পারে, ঘটিবেও। আজ কিছু হইল না বটে, কিন্তু কাল নিশ্চয় হইবে। প্রত্যেকদিন সকালে উঠিয়াই আনন্দে মন ভরিয়া যায়, নতুন সম্ভাবনা লইয়া আর একটি দিন শুরু হইল। বাতাসে সমুদ্রপারের মশলাদ্বীপ হইতে ভাসিয়া আসা সুগন্ধ, চেতনায় মুক্তির সুর।
সময় কাটিতে আরম্ভ করিলে জীবনের এই পট বদলাইতে থাকে। দায়িত্ব, কর্তব্য, ছকে বাঁধা সময়সুচি আর বহুবিধ সমস্যা আসিয়া পূর্বের সরল আনন্দকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। বাতাস আর তেমন করিয়া বয় না, আকাশের নীল বিবর্ণ হইয়া আসে। নদীর স্রোতের শব্দে আর আগের মতো প্রকৃতির রহস্যময় গোপন সংগীত বাজে না। সে বড়ো ভয়ের সময়, বড়ো কষ্টের সময়।
কাজলের এখন সেই বয়েস। যন্ত্রণা একা সহ্য করিতে হয়, সব সমস্যায় দৌড়াইয়া মায়ের কাছে আসিয়া পরামর্শ চাওয়া যায় না, অনেক সমস্যার কোন উত্তরই থাকে না। ছোটবেলার বিশ্বাস, প্রথম যৌবনের মূল্যবোধ, আজীবন সঞ্চিত যা কিছু ভালোলাগার সম্পদ—সব একে একে বদলাইয়া যায়। চেনামুখ সরিয়া যায়, অচেনা মুখ নতুন বন্ধুত্ব লইয়া আসে না—এ বড়ো কঠিন সময়।
তুলিকে সে ফেলিতে পারিবে না। তুলির সঙ্গে তাহার আজ পর্যন্ত একটাও এমন কোন কথা হয় নাই, যাহাকে মন দেওয়া-নেওয়ার ভূমিকা বলা যাইতে পারে। আর দেরি করা যায় না, অপালার প্রতি তাহার আচরণ একান্ত নিষ্ঠুর হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু তুলিকে স্বীকৃতি না দিলে আরও বেশি অন্যায় করা হইবে। অপালা উচ্চশিক্ষিতা, প্রতিপত্তিশালী পিতার সুন্দরী কন্যা, তাহার ভালো বিবাহ হইতে সময় লাগিবে না। কিন্তু তুলির কেহ নাই, বিমলেন্দুর বয়েস হইয়া আসিতেছে, তিনি আর কতদিন ভাগ্নীকে দেখিবেন? মায়ের কলঙ্কের জন্য কেহ তাহাকে বিবাহ করিতে রাজি হইবে না। বাঙালি সমাজে এসব কথা চাপা রাখা কঠিন, নির্যাতন করিতে পারিলে মানুষ আর কিছু চায় না।
সরল তুলি-জীবনের বিরুদ্ধ স্রোতের তীব্রতায় কোথায় ভাসিয়া যাইবে।
আচ্ছা, এমনও তো হইতে পারে যে, সে এত চিন্তা করিতেছে, কিন্তু তুলি তাহাকে পছন্দ করিবে না? সব মেয়েরই মনে স্বামী সম্বন্ধে একটা ভাবমূর্তি থাকে। তুলির কল্পনার সঙ্গে তাহার ব্যক্তিত্ব হয়তো একেবারেই মেলে না। বিমলেন্দুর ব্যবস্থা সে হয়তো নীরবে মানিয়া লইবে, কিন্তু বিবাহিত জীবনে সুখী হইবে না।
কী করা যায়? সে কি সংকোচ কাটাইয়া সরাসরি তুলির সঙ্গে কথা বলিবে? নাঃ, সে তাহা পারিবে না। চিঠি লিখিয়া মন জানিতে চাহিবে? না, তাহাও বড়োই নাটকীয় হইয়া যাইবে। অবশ্য এমনি একবার দেখা করিতে যাওয়া যায়। কে কেমন আছে জানিতে যাওয়াটা এমন অন্যায় কিছু নয়।
অনেক ভাবিয়া সে যাওয়াই ঠিক করিল।
তবে সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝিতে পারিল যে, কেবলমাত্র কুশল প্রশ্ন করিবার আগ্রহে সে ছুটিয়া যাইতেছে না। নমুখী এক সুন্দরী তরুণীর সহিত দেখা হইবার সম্ভাবনা তাহাকে প্ররোচিত করিতেছে। অবশ্য তাহাতে কিছু আসে-যায় না, নিজের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করিয়া কী লাভ? সে যে তুলিকে ভালোবাসিতে শুরু করিয়াছে ইহাতে তত সন্দেহ নাই।
সিদ্ধান্ত লইবার পরদিনই কাজল খুব সকালের ট্রেনে কলিকাতায় রওনা হইল। বিমলেন্দুর বাড়ি পৌঁছাইয়া দেখিল তিনি বাহিরের ঘরে বসিয়া স্টেটসম্যান পড়িতেছেন। তাহাকে দেখিয়া বিমলেন্দু যথার্থই খুশি হইলেন, বলিলেন–তোমার খবর কী হে? কলকাতায় আর আসছ না নাকি, মা কেমন আছেন?
যথাবিহিত কুশল বিনিময়াদির পর বিমলেন্দু বলিলেন—এত সকালে এসেছ মানে নিশ্চয় কিছু খেয়ে বের হওনি? দাঁড়াও, তোমার জলখাবারের ব্যবস্থা করি। এমনি কি বিশেষ কোনো কাজ আছে কলকাতায়? নেই? তাহলে দুপুরেও এখানে খেয়ে একেবারে ওবেলা যাবে। কী ভালোবাসো বলমাংস না মাছ? আমি নিজে তোমার জন্য বাজার করব
কাজল বাধা দিবার চেষ্টা করিল, বলিল—অকারণে বাজারে ছুটির প্রয়োজন নাই, বাড়িতে যা আহে তাহই যথেষ্ট।
বিমলেন্দু সে-সবে কর্ণপাত করিলেন না, গলা উঠাইয়া ডাকিলেন-তুলি! তুলি!
কাজলের বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। এইবার দেখা হইবে—এইবার তুলি আসিবে।
একখানি বেগুনী রঙের শাড়ি পরনে, মামার ডাকে তুলি আসিয়া ঘরে ঢুকিল।
সামাজিকতা ভূলিয়া কাজল অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিল।
এই সকালেই তুলির স্নান সারা হইয়া গিয়াছে। ভেজা চুল পিঠের উপর বিন্যস্ত। মুখে কোনো প্রসাধনের চিহ্ন নাই, তবু তুলিকে দেবীর মতো দেখাইতেছে। বাবার ডায়েরিতে তুলির মায়ের কথা কাজল পড়িয়াছে। মেয়েকে দেখিলে মায়ের সে সৌন্দর্য আন্দাজ করিতে পারা যায়।
তুলির মা সুখী ছিলেন না, মেয়েরও কি সেই ভাগ্যই হইবে?
না, তুলিকে সে সমস্ত কষ্ট হইতে রক্ষা করিবে। তাহার গায়ে রৌদ্র লাগিতে দিবে না।
বিমলেন্দু বলিলেন–তোমার ইয়ে, কী বলে—অমিতাভদা এসেছেন। চট করে কিছু লুচি ভেজে দাও।
কাজল বলিল—কেমন আছো তুলি? আর দুর্বলতা নেই তো?
তুলি হাসিয়া বলিল—ভালো আছি। আপনারা কেমন আছেন? মা?
কাজলের ভালো লাগিল, তুলি মাসিমা বা কাকিমা বলিয়া হৈমন্তীকে নির্দেশ করিল না, একেবারে মা বলিয়া ডাকিল। চেহারায় আচরণে এমন কমনীয় মেয়ে সে আর কখনও দেখে নাই।
জলখাবার তৈরি করিবার জন্য তুলি বাড়ির ভিতরে গেলে বিমলেন্দু তাহার সঙ্গে সাহিত্য, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ইউ.এন.ও-র অপদার্থতা, সেকালে সবকিছুই ভালো ছিল ইত্যাদি লইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। কাজল বলিল—সে কী মামা, পৃথিবীসুদ্ধ লোক ইউ এন.ও. নিয়ে এত মাতামাতি করছে, আর আপনি বলছেন ও দিয়ে কোনো কাজ হবে না!
–হবে না তো! তুমি মিলিয়ে দেখে নিয়ে আমার কথা খাটে কিনা। লীগ অফ নেশনস হবার পরে কেউ কি আর ভেবেছিল আরও একটা মহাযুদ্ধ হবে? আসলে মানবজাতির চবিত্রের মধ্যে বর্বরতার বীজ আছে। সভ্যতার পালিশ দিয়ে আমরা সেটা ঢেকে রাখি মাত্র। সে পালিশটাও খুব হালকা, মাঝে মাঝেই নিচের কালো রঙটা বেরিয়ে পড়ে। যুদ্ধ আবার হবেই, আজ না হোক বিশ পঞ্চাশ কী সত্তর বছর পরে হলেও হবে। আর ছোটখাটো ঘরোয়া ক্ষেত্রে তো যুদ্ধ চলছেই, তাই না? সংসারে কর্তৃত্বের জন্য, অফিসে ক্ষমতা আর পদোন্নতির জন্য, রাজনীতিতে সর্বশক্তিমান হবার জন্য, যে কোনো উপায়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবার জন্য যুদ্ধ চলছেই। এসবই বাড়তে বাড়তে একদিন বৃহৎ আকারে ফেটে পড়ে।
কাজল বলিল—ইউনাইটেড নেশনস ব্যর্থ হবে বলছেন, তাহলে মানুষের বাঁচবার উপায় কী?
বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া বিমলেন্দু বলিলেন—লোভ ত্যাগ করা। অল্পে সন্তুষ্ট থাকা।
–তাহলে তো জ্ঞান-বিজ্ঞান, কল-কারখানা, সভ্যতার অগ্রগতি সব থেমে যাবে। লোভই বলুন আর যাই বলুন, মানুষ নিজের অবস্থার আরও উন্নতি ঘটাতে চায় বলেই বিজ্ঞানের আবিষ্কার ঘটে, দেশ এগিয়ে যায়
–না, সম্পূর্ণ ভুল। কল-কারখানা বা ঐশ্বর্য দিয়ে সভ্যতার অগ্রগতি মাপা যায় না, সেটা মাপা হয় সংস্কৃতির মান দিয়ে। শেকীয়ার কিংবা কালিদাস অথবা ব্যাসদেবের সময়ে প্রযুক্তি তার শৈশবে ছিল, কিন্তু তাদের কীর্তি নিয়েই তো আমরা গর্ব করি, গবেষণা করি। আমি বলছি না যে বিজ্ঞানচর্চা ছেড়ে দাও, প্রযুক্তি থামিয়ে দাও—আমি বলছি এ ধরনের উদ্যোগকে একটা সীমার মধ্যে আরদ্ধ রাখো। ভোগের তৃষ্ণা বাড়ালেই বাড়ে, সময়মত না থামালে সর্বনাশ!
তুলি এই সময়ে জলখাবার লইয়া আসায় বিমলেন্দুর বক্তৃতাস্রোতে বাধা পড়িল। তিনি উঠিয়া একটা জামা গায়ে গলাইতে গাইতে বলিলেন–তুমি বসে তুলির সঙ্গে কথা বলে, আমি চট করে একবার বাজার থেকে ঘুরে আসি। তুলি, দেখিস ওর আর কী লাগে—
কাজলের আপত্তিতে কর্ণপাত না করিয়া বিমলেন্দু ব্যাগ হাতে বাহির হইয়া গেলেন।
সুচি খাইবার মতো মনের অবস্থা কাজলের ছিল না। সে মাথা নিচু করিয়া খাবার নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। তুলনায় তুলির আচরণ অনেক সহজ, কারণ শৈশব হইতে যেভাবে সে বড়ো হইয়াছে তাহাতে লজ্জার বোধ জন্মাইবার কোনো সুযোগ ছিল না। মামাকে ছাড়িয়া দিলে কাজল তাহার জীবনে প্রথম পুরুষ যাহার সঙ্গে বসিয়া সে একান্তে কথা বলিতেছে। লজ্জা করিতে সে শেখে নাই, কিন্তু তাহার ন, একান্ত মেয়েলি স্বভাব তাহাকে অনন্য করিয়া তুলিয়াছে।
মাথা নিচু করিয়াই কাজল বলিল—তুলি, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে,
বাড়ি খালি, ফিসফিস করিয়া কথা বলিবার কোনো প্রয়োজন নাই, তবু গোপন ষড়যন্ত্র করিবার সময় মানুষের কণ্ঠস্বর যেমন খাদে নামিয়া যায়, কাজলের গলাও তেমনই শুনাইল। এই পরিবেশে অমনভাবে কথা বলিলে তাহার একটিই অর্থ হয়। কিন্তু তুলি তো পূর্ণ নারীত্বে পৌঁছায় নাই। সে কাজলের মুখের দিকে নিঃসংকোচ দৃষ্টি রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আমার সঙ্গে? কী কথা?
এবার কাজল মুখ তুলিল, গলা পরিষ্কার করিয়া বলিল—তোমার মামা এখন বাড়ি নেই, এভাবে একথা বলা উচিত হচ্ছে কিনা জানি না। কিন্তু কথাটা কেবল তোমাকেই বলবার মতো, আর কেউ সামনে থাকলে বলা যাবে না। মনোযোগ দিয়ে শুনে তোমার উত্তর দাও
এইবার বোধহয় পরিস্থিতি তুলি কিছুটা বুঝিল। মেয়েদের স্বাভাবিক উপলব্ধির ক্ষমতা দিয়া সে বুঝিল তাহার জীবনের সম্পূর্ণ নূতন এক পর্বের প্রস্তাবনা হইতে চলিয়াছে। একটু একটু করিয়া তাহার মুখে অরুণাভা ছড়াইয়া পড়িল। এইবার সেও ফিসফিস করিয়া বলিল—বলুন!
–তুমি তো জানো, তোমার মা আর আমার বাবা বন্ধু ছিলেন। হয়তো এই বন্ধুত্ব আরও গভীর সম্পর্কের দিকে গড়াতো, কিন্তু আমার বাবা দরিদ্র ছিলেন, খুবই সাধারণ অবস্থার মানুষ দুবেলা তার খাওয়া জুটতো না। তোমরা ছিলে বড়ো ঘব, তোমার মা রাজার ঐশ্বর্যের মধ্যে বড়ো হয়েছেন। ছোটবেলায় বন্ধুত্ব হতে হয়, কিন্তু তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। শেষপর্যন্ত তোমাদের বাড়ির দিক দিয়ে কেউ ব্যাপারটা মেনে নিতো না। অবশ্য সে প্রশ্নও ওঠে না, কারণ খুব অল্পবয়েসেই বাবা আমার ঠাকুমাব সঙ্গে তোমাদের বাড়ি ছেড়ে মনসাপোতায় চলে যান। আই.এ পাস করার পর অদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাবার বিয়ে হয়। সে গল্প হয়তো তোমার মামার কাছে তুমি শুনে থাকবে। তোমার মায়েরও বিয়ে হয়ে যায়। আমাকে জন্ম দিতে গিয়ে আমার মায়ের মৃত্যু হয়। মা বলতে আমি এই মাকেই জানি, তিনিও সন্তান বলতে আমাকেই জানেন।
কাজল একটু থামিল। তুলি পূর্ণদৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া আছে।
—তোমার মায়ের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বাবার সঙ্গে তার সম্পর্ক খুব মধুর ছিল, ঘনিষ্ঠ ছিল। এ যে কত পবিত্র ঘনিষ্ঠতা তা আমি বলে বোঝাতে পারবো না। দুজনে পরস্পরের নিঃসীম একাকীত্বকে গভীর আত্মিক সান্নিধ্য দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছিলেন। তোমার ছোটবেলায় ভবানীপুরের বাড়িতে বাবা তোমাকে প্রথম দেখেন-তখন তোমার মা মারা গিয়েছেন। তোমাকে দেখে সেই রাত্তিরেই বাবা তার ডায়েরিতে একটা ইচ্ছের কথা লিখে যান—সে ইচ্ছে তোমাকে আর আমাকে ঘিরে।
কাজল আবার থামিল। মরিয়ার মতো অনেক কথা বলিবার পর তাহার বুক ঢিপ ঢিপ করিতেছে। তুলি কি কিছু মনে করিল? সে কি ভাবিতেছে যে, নির্জন বাড়িতে একা পাইয়া কাজল তাহাকে অন্যায়ভাবে প্রভাবিত করিবার চেষ্টা করিতেছে? খুব অস্পষ্ট স্বরে তুলি বলিল—এসব আমি কিছুটা জানি। আপনি কী বলবেন?
তুলির কথায় কাজল অবাক হইল, বেশ ভালোও লাগিল। তুলি সরল, ন; কিন্তু তাহার আড়ষ্টতা নাই–সে বোকাও নয়। ঠিক কথা ঠিক সময়ে বুঝিতে পারে।
কাজল বলিল—তুমি কী করে জানলে? কে বলেছে তোমাকে?
–মামা। মানে ঠিক ওভাবে বলেন নি, তবে মাঝে মাঝেই নানা কথায় আমি বুঝতে পারছিলাম এমন একটা কিছু ঘটতে চলেছে।
কাজলের গলার কাছে কী একটা গুটলি পাকাইয়া উঠিতেছে। তুলির শরীর হইতে কেমন একটা মৃদু সুগন্ধ পাওয়া যায়, তার সবটাই এসেন্স নহে, তরুণী-শরীরের নিজস্ব ঘ্রাণ–রৌদ্রের গন্ধের মতো, বৃষ্টিভেজা কদমের গন্ধের মতো, শাশ্বতী মানবীর মতো।
সে বলিল—এমন কিছু ঘটলে তোমার কি আপত্তি হবে?
এবার তুলি চুপ করিয়া রহিল।
কাজল বলিল–চুপ করে থাকলে তো চলবে না, মামা এসে পড়ার আগে তোমার মতটা আমার জানা প্রয়োজন। তাহলে আমিও ওঁর সঙ্গে কথা বলে যাব।
—আমার মত জানা কেন প্রয়োজন?
–কারণ তুমি খেলার পুতুল নও যে, দোকান থেকে পছন্দ করে কিনে নিয়ে যাব। তাছাড়া আমার বাবা চেয়েছিলেন বলেই এতে তোমারও মত থাকবে তার কী মানে আছে? যাক, এসব ছেড়ে দিলেও তোমার দিক থেকে আরও অনেক ভাববার বিষয় থেকে যায়—
—কী?
—যেমন ধরো, আমার বাবার খ্যাতি আছে সত্য, কিন্তু আমরা বড়োলোক নই। তুমি অভিজাত ধনী পরিবারের মেয়ে, তুমি মানিয়ে নিতে পাববে তো? এ তো দুদিনের খেলা নয়, সারাজীবনের মতো সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তোমার কী মত? ভেবে বলো—
তুলি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল, তাবপব আস্তে আস্তে বলিল–বাবা যা ঠিক কবে গিয়েছেন, তার ওপরে আমার আর বলাব কী আছে?
কাজলের সমস্ত শবীরে একটা কেমন ভালো লাগার, তৃপ্তির শিহরণ বহিযা গেল। সে বুঝিল তাহার বাবাকে তুলিও বাবা বলিয়া উল্লেখ কবিতেছে। তবু সে বলিল–না, আরও ভাববার কথা আছে।
–কী?
–আমার বলতে সংকোচ হচ্ছে, তুমি হয়তো ব্যাপারটা জানো, তবু একবার নিজের মুখে না বলে নিলে আমি শান্তি পাবো না
তুলি বিস্মিত চোখে তাকাইয়া বলিল—কী বলবে তুমি? আমি বুঝতে পাবছি না—
—দেখ, আমার ঠাকুমা সর্বজয়া দেবী, তোমাদের বাড়িতে—
কাজল থামিয়া গেল। তুলি অপলকে তাকাইয়া আছে।
মনের জোর সংগ্রহ করিযা কাজল বলিল—আমার ঠাকুমা তোমাদের বাড়িতে রাঁধুনির কাজ করতেন। আমাকে বিয়ে করলে তোমার সম্মানে আঘাত লাগবে না তো?
এইবার যাহা ঘটিল তাহা সত্যই বিস্ময়জনক। কাজল এতদিন তুলিকে নিতান্ত লাজুক আর স্বল্পভাষিণী বলিয়া ভাবিয়া আসিয়াছে, কিন্তু প্রয়োজনের সময় মেয়েবা যে কত সরল অথচ বলিষ্ঠভাবে নিজের কথা বলিতে পারে তাহা সে আজ দেখিল।
তুলি তাহার দিকে তাকাইয়া বলিল—যুধিষ্ঠির বিরাটরাজের চাকরি স্বীকার করেছিলেন, ভীম রাঁধুনির কাজ করতেন, দ্রৌপদী রানীর পরিচারিকা চিলেন। তাঁরা কি সম্মানে কারও চেয়ে কম ছিলেন? অবস্থায় রকমফের সবারই হয়, তার জন্য মানুষ ছোট হবে কেন? আজ বাবার যে দেশজোড়া খ্যাতি, মানুষ তাকে উপনিষদকাব ঋষির সঙ্গে তুলনা করছে, সে খ্যাতি আর সম্মানের কাছে জমিদারির গর্ব দাঁড়াতে পারে? আজ কোথায় আমাদের সে জমিদারি? কোথায় সে সম্মান? আর বাবাকে দেখ, তিনি সবাইকে ছাড়িয়ে মাথা তুলে উঠেছেন।
তারপর একটু হাসিয়া বলিল—আচ্ছা আমি তোমাদের রাঁধুনি হয়ে সবকিছু শোধবোেধ করে দেব, তাহলে হবে তো?
বিমলেন্দু বাজার হইতে ফিরিলেন। তুলি উঠিয়া রান্নার জোগাড় দেখিতে গেল। অন্যমনস্ক কাজল অনেকক্ষণ বাদে খেয়াল করিল তুলি তাহাকে কখন যেন তুমি সম্বোধন করিতে শুরু করিয়াছে। কখন হইতে এটা ঘটিল? সে খেয়াল করে নাই তো!
সারাদিনে তুলির সঙ্গে আর বিশেষ কথা হইবার সুযোগ হইল না। খাওয়া সারিয়া বিমলেন্দু কাজলকে লইয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিলেন এবং ক্রমাগত একালের দোষ ও সেকালের গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। কোনো কোনো প্রসঙ্গে কাজল তাহার সহিত একমত হওয়া সত্ত্বেও সে আলোচনায় যোগ দেওয়ার উৎসাহ পাইল না।
মাথার মধ্যে যেন কেমন করিতেছে। অথবা ঠিক মাথার মধ্যে নয়, সমস্ত চেতনায় কেমন একটা অস্থিরতার ভাব।
অনেকদিন আগে, তাহার বাবার কৈশোরে যে নাটক শুরু হইয়াছিল, এতদিনে বোধহয় তাহা স্থির পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। মৃত্যুর ওপারের জগৎ হইতে তাহার বাবা ও তুলির মা নিশ্চয় তৃপ্তিলাভ করিবেন। নিজেদের বিচ্ছেদ সন্তানের মিলনে পূর্ণতা লাভ করিবে। মহাকালের কী বিচিত্র গতি।
বিকালে বিদায় লইবার সময় সে বিমলেন্দুকে বলিল—মামা, আপনি একবার আমাদের বাড়ি যাবেন না?
বিমলেন্দু বলিলেন–হাঁ, সে তো যাবো নিশ্চয়। দেখি এইবার–
হঠাৎ থামিয়া তিনি তীক্ষ্ণচোখে কাজলের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—তুমি কি—মানে, বিশেষভাবে যাওয়ার কথা বলছো?
মাথা নিচু করিয়া কাজল বলিল–আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি আপনার কাছ থেকে ভেবে দেখবার জন্য সময় চেয়ে নিয়েছিলাম, আমি মনস্থির করে ফেলেছি, এবার আপনি একবার চলুন—
বিমলেন্দুর মুখ দেখিয়া মনে হইল তিনি আগেই আন্দাজ করিয়াছিলেন, কাজল আজ এই কথা বলিবে। তিনি বলিলেন—তোমার মা?
-মায়ের অমত হবে না।…
বিমলেন্দু চুপ করিয়া একমুহূর্ত কী ভাবিলেন, তারপর বলিলেন—আমার দিদির জীবনের সব কথা কি তোমার মা ঠিকঠাক জানেন? সমাজ খুব হিংস্র অমিতাভ, মানুষ মানুষকে পীড়ন করে বড়ো সুখ পায়। বিয়ের পর যদি কেউ এসব পুরোনো কথা দিয়ে ঘাটাঘাটি করে।
কাজল বলিল—আমার মা সব জানেন। সমাজকে তিনি মানেন, কিন্তু সমাজের অন্যায় আচরণকে ভয় পান না। তাছাড়া বাবা যাকে সমর্থন করে গিয়েছেন, সে কাজ করতে মায়ের কোনো দ্বিধা হবে না। ও নিয়ে চিন্তা করবার কারণ নেই।
বিমলেন্দুর মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—আমি যাব, খুব শিগগীরই যাব, তোমার মাকে বোলো। অমিতাভ, তুমি যে আমাকে কতবড় দায় থেকে উদ্ধারের আশা দিলে, তা আমি কী করে বোঝাবো? পিতার উপযুক্ত সন্তান তুমি, তোমার মঙ্গল হোক—
ছুটির দিনের সন্ধ্যার ট্রেনে বেশি ভিড় নাই। জানালার ধারে বসিয়া কাজল বাহিরে তাকাইয়া ছিল। একটু একটু করিয়া অন্ধকার নামিতেছে, ঝোপঝাড় বাড়িঘর সস পিছাইয়া যাইতেছে।
কাজলের মন এক বিচিত্র অনুভূতিতে ভরিয়া উঠিল। কবেকার ফুরাইয়া যাওয়া আতরের শিশি খুলিলে যেমন অস্পষ্ট সুগন্ধের রেশ মনকে উদাস করে, তেমনি তাহাদের পরিবারের ইতিহাস, তাহার বাবার পুণ্যস্মৃতি, তুলির মায়ের ব্যর্থ জীবন, নিশ্চিন্দিপুর আর মৌপাহাড়িতে কাটানো তাহার স্বপ্নের শৈশব–সমস্ত তাহার চেতনার পটে একসঙ্গে ভাসিয়া উঠিল।
বাবা যদি বাঁচিয়া থাকিত।
কত কথা বলিতে ইচ্ছা করে, ছোটবেলার মতো চুপ করিয়া বাবার পাশে শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু উপায় নাই। নির্মম মহাকাল তাহার বাবাকে কোন অজানা দেশে লইয়া গিয়াছে। বাবা এখন কেবলমাত্র অতীতের এক সুখস্মৃতি।
কিংবা সত্য কি তাই? বাবাকে কি সে প্রতিমুহূর্তে নিজের রক্তের ভিতর, চেতনা ও উপলব্ধির ভিতর অনুভব করিতেছে না? বাবার চাইতে তাহার কাছে আর কে বেশি করিয়া জীবিত?
মায়ের শরীর ভালো নয়। তুলি আসিয়া মাকে যত্ন করিবে, মায়ের হাত হইতে কাজ তুলিয়া লইবে। সামনে কঠিন কাজ আসিতেছে, বাবার স্মৃতিরক্ষার কাজ, সেই কাজে তাহাকে সাহায্য করিবে। যে কাজ প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ, একান্ত আপন ছাড়া তাহাতে কেহ সহায়তা করিতে পারে না।
একজন খুব কষ্ট পাইবে। সবদিক দিয়াই সে বঞ্চিত হইল।
বাহিরে অন্ধকারে চাহিয়া কাজল মনে মনে তাহার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। সেদিন রাত্রে She walks in beauty, like the night পড়িতে পড়িতে ঘুম আসিল। আলো নিভাইবার পর ঘুমাইয়া পড়িবার আগে পর্যন্ত যে স্তিমিত চেতনার রাজত্ব, সেইখানে কাজলের মন সামান্য সময়ের জন্য দাঁড়াইয়া গেল।
ঈর্ষা, যুদ্ধ, লোভ আর মৃত্যুর সীমাবদ্ধতার পরপারে অনন্ত শূন্যের ভিতর দিয়া সৌরবাতাস বহমান। বিশ্বের ইতিহাস মেসোপটেমিয়া, শানিদার গুহাবাসী নিয়ানডার্থাল কিংবা জলচর ট্রাইলোবাইটদের সিরিয়ান যুগে শুরু হয় নাই, পৃথিবীর জন্মেরও আগে-নক্ষত্রদের জন্মের আগে, নক্ষত্ৰ-নীহারিকা,মহাশূন্য-মহাকাল যখন একটিমাত্র বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত সম্ভাবনা হিসাবে বিরাজমান ছিল, ইতিহাসের প্রথম পাতা তখন লেখা হইয়াছে। বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে মানুষ আসিয়াছে এই সেদিন, কিন্তু সৃষ্টির সেই আদিম মুহূর্ত হইতে চরাচরব্যাপী এক মহাচেতনা দেশকালে ব্যাপ্ত হইয়া ছিল। তাহা হইতেই জগৎ, তাহা হইতেই যাবৎ বস্তুপিণ্ড। প্রেম, কবিতা, দর্শন, বিজ্ঞান—যে ছোট ফুলটি সুবর্ণবেখার তীরে সে ঘাসের মধ্যে ফুটিয়া থাকিতে দেখিয়াছে, সেটি হইতে দূর ভবিষ্যতে সময়ের শেষ ভগ্নাংশ পর্যন্ত সমস্ত কিছু সৃষ্টিপূর্ব ওই মহাচেতনাব মধ্যে লুকাইয়া ছিল।
তুলির সঙ্গে তাহার যোগাযোগ সেই বিশ্ব-পরিকল্পনারই অংশ। আকস্মিক নহে নির্ধারিত।
ঘুম আসিবে—ঘুম আসিতেছে।
কোথায় যেন এক বিস্তৃত শাল-পিয়াশাল-অর্জুনের বন। সে বনের মাথায় পূর্ণিমার চঁদ উঠিয়াছে। রাতজাগা পাখি ডাকিতেছে কোথায়। দক্ষিণ হইতে আসা বাতাসে শুষ্কপত্র মর্মরশব্দে সরিয়া যাইতেছে। গানের সুর জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিকে উতলা করিয়াছে। অজানা অদ্ভুত এক সুর, পৃথিবীর সব মানুষই সে সুর শুনিয়াছে। আন্তনাক্ষত্রিক শূন্যে সঞ্চরমাণ নীহারিকাদের সে সংগীত। যে শুনিয়াছে, ঘরে আর তাহার মন বসে না। প্রথম যৌবনে আকাশের দিকে তাকাইয়া সেই আদিম রহস্যময় সুর সে একবার শুনিতে পাইয়াছিল, তাই অল্পে সে আর ভোলে নাই। হয়তো এবার আর কিছু হইল না, এ জন্মটা হয়তো বৃথাই গেল, কিন্তু তাই বলিয়া সে নকল সোনা কিনিতে যায় নাই। যেখানে থাকুক, যাহাই করুক, বুকের পাঁজরে সেই অনির্বাণ সংগীত বাজিয়াছে।
ওই জ্যোৎস্নালোকিত অরণ্যভূমির প্রসার পার হইয়া কে যেন তাহার দিকে আসিতেছে।
কে? অপালা? তুলি? তাহার না-দেখা হারানো মা?
না, যে আসিতেছে তাহাকে সে চেনে না। সমস্ত সৃষ্টির নির্যাস লইয়া ইহার অবয়ব। সে মানব নয়, মানবীও নয়, পৃথিবীর কোনো পরিচিত আকারের স্বীকৃত মাত্রায় ইহাকে ধরা যায় না।
কাজলের জাগতিক চেতনা তখন প্রায় নিদ্রাকে স্পর্শ করিয়াছে। তবু তাহার গায়ে শিহরণ জাগিল। যে আসিতেছে তাহারই জন্য কাজলের এতদিনের অপেক্ষা ছিল। এতদিনে আসিল তবে।
কিন্তু চিরপ্রার্থিত সেই মুহূর্তটি শেষ পর্যন্ত আসিল না। যে আসিতেছিল, সে মানুষের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর লইয়া পরম সার্থকতা হিসাবে আসিতেছিল। সে পৌঁছাইবার ঠিক আগেই কাজল ঘুমাইয়া পড়িল।
সুপ্তির প্রান্ত হইতেই শুরু হয় স্বপ্নের অধিকার।
ঘুমাইয়া কাজল সেই রাত্রে অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখিল। যে গ্রহণ করিতে জানে প্রকৃতি তাহাকেই গ্রাহ্যবস্তু দেন। কাজলের সংবেদনশীল মন জীবনের প্রধান এক বাঁকে আসিয়া আরও সংবেদী হইয়া উঠিয়াছিল। স্বপ্নের জগতে সত্যকে যুক্তির জাল দিয়া ধরিতে হয় না, সত্য প্রকাশ ও সম্পূর্ণ হইয়া আপনিই ধরা দেয়। স্বপ্নের মধ্যে কাজল সমস্ত বস্তুবিশ্বকে কী এক জাদুবলে একসঙ্গে দেখিতে পাইল। সেখানে কশা কশা হাইড্রোজেন সঞ্চিত হইয়া আলোকবর্ষব্যাপী নীহারিকার সৃষ্টি হইতেছে, নীহারিকার গর্ভে জন্ম লইতেছে নক্ষত্রের দল। সীমাহীন শূন্যে জ্যোতিষ্কেরা বিশাল দূরত্বের ব্যবধানে ভ্রাম্যমাণ।
আর সেই নক্ষত্রের কেন্দ্রে আবির্ভূত হইতেছে জীবনের মৌলকণা। যে পদার্থে তাহার শরীর গঠিত, নদী পাহাড় বনস্পতি ও সমগ্র জীবজগৎ গঠিত, সেই বস্তুপুঞ্জ সমস্ত বিশ্ব হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহার শরীরে মিলাইয়া যাইতেছে।
মহনীয়, উদার অনুভূতিতে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। সে নক্ষত্রের সন্তান, মরণশীলতা দ্বারা তাহার জীবন সীমাবদ্ধ নয। সে মহাবিশ্বের তাৎপর্যবাহী অধিবাসী, সে নক্ষত্রের সন্তান।
শীতের শেষে সে বৎসর বসন্ত আসিল একখানি গীতিকবিতার মতো।
হিমের আড়ষ্টতা ভাঙিয়া সমস্ত জগৎ যখন নতুন প্রারম্ভের ভূমিকা হিসাবে কচি পাতায় আর দক্ষিণ হইতে আসা বাতাসে নিজেকে প্রকাশ করিতেছে, তেমনই এক দিনে হৈমন্তী কলিকাতায় গিয়া তুলিকে আশীর্বাদ করিয়া আসিল। সঙ্গে গেল প্রতাপ আর পরিবারের বন্ধু দু-একজন। বিবাহ হইবে আষাঢ়ের একত্রিশ তারিখে। উভয়পক্ষেরই লোকবল কম, প্রস্তুতির জন্য এই সময়টা প্রয়োজন।
আশীর্বাদের আগের দিন রাত্রে হৈমন্তী একবার কাজলের ঘরে গেল। সকাল সাতটার মধ্যে পুরোহিতের আসা প্রয়োজন, না হইলে ট্রেন ধরা যাইবে না। পুরোহিত মশাইকে খবর দেওয়া হইয়াছে তো?
ছেলের ঘরে ঢুকিয়া হৈমন্তী দেখিল কাজল ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। টেবিলের ওপর একটি পুরানো, প্রায় মলাট-ছেঁড়া অ্যালবাম আর কাজলের ডায়েরিখানা। অ্যালবামটি সে চেনে, অপুর উদাসীন, ভবঘুরে জীবনের ঘূর্ণি হইতে রক্ষা পাওয়া কিছু ছবি তাহাতে আছে।
কিন্তু বিশেষ করিয়া আজই এটি ছেলের টেবিলে কেন?
হৈমন্তী সামান্য ইতস্তত করিয়া অ্যালবাম খুলিল।
প্রথম পাতাতেই অপর্ণার একখানি ছবি কেবলমাত্র মুখ ও গলার খাজ পর্যন্ত ছবিতে দেখা যাইতেছে, দৈর্ঘ্যে বারো ইঞ্চি, প্রস্থে দশ ইঞ্চির এনলার্জমেন্ট।
হৈমন্তীর বুকের ভেতরটা একবার টনটন করিয়া উঠিল। সে সব জানিয়া, সব মানিয়াই বিবাহ করিয়াছিল। প্রথমা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আমৃত্যু গভীর ভালোবাসার কথা সে যে জানে না এমন নয়। তবু মন-কেমন করে। অপর্ণার প্রতি তাহার কোন ঈর্ষা নাই, স্বামীর অনির্বাণ ভালোবাসার জন্য কোন ক্ষোভ নাই—তবু মন-কেমন করে। ভাগ্যের অনিবার্যতায় স্বামীকে সে সম্পূর্ণ নিজের করিয়া পায় নাই। তাহার দেবতার মতো স্বামী, কোনদিন কষ্ট দেয় নাই, তাহার মন খারাপ হইতে পারে ভাবিয়া কখনও অপর্ণার প্রসঙ্গ তোলে নাই, স্বামীকে হৈমন্তী কোন দোষ দিতে পারিরে না। কিন্তু মেয়েদের মন বড়ো অদ্ভুত, বিচিত্র। আজ ছেলের টেবিলে মায়ের ছবি দেখিয়া অকস্মাৎ হৈমন্তী আবিষ্কার করিল অপর্ণা এই সংসারে এখনো পরিপূর্ণভাবে জীবিত। কাজল তাহার বিবাহের আশীর্বাদের আগের দিন মায়ের ছবি দেখিতেছিল, ডায়েরিতেও নিশ্চয় মায়ের কথা লিখিয়াছে। একটু ইচ্ছা হইলেও সে নিজেকে সংযত করিল। না, ছেলের ডায়েরি সে পড়িবে না।
স্বামীর মতো ছেলেও। শৈশব হইতে যাহাকে নিজের অপূর্ণ মাতৃত্বের বঞ্চনা ভুলিয়া মানুষ করিয়াছে, সেও সম্পূর্ণ নিজের হইল না, অর্ধেক আরেকজনের রহিল।
কাল তুলির আশীর্বাদ। কিছুদিন পরেই এ সংসারে একজন বহিরাগত আসিবে। অন্য কিছু না, নিজের ওপর তাহার বিশ্বাস আছে, সে নিশ্চয় যে কোনো অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিবে, কিন্তু ছেলের ওপর যে অর্ধেক অধিকার তাহার ছিল, আবার তাহার অর্ধেক আর একজনকে ছাড়িয়া দিতে হইবে।
ছাড়িয়া দেওয়াই নিয়ম। ছাড়িয়া দেওয়াই তো উচিত।
সব ঠিক ঠিক, সব যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু তাহার শেষ সম্বলটুকুরও অর্ধেক ছাড়িয়া দিতে হবে। কাজল একাধারে তাহার ছেলে ও স্বামীর প্রতিনিধি। যদি সবটাই ছাড়িতে হয়?
এমন তো হয় সে শুনিয়াছে। তাহারও হইবে না তো?
আশঙ্কায় তাহার বুকের ভিতরটা কেমন হিম হইয়া গেল!
পরক্ষণেই ছেলের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকাইয়া তাহার সুপ্ত মাতৃত্ব স্নেহের স্তন্যধারায় উৎসারিত হইয়া উঠিল। না, তাহার ছেলে তাহাকে ভুলিবে না। তেমন হইতেই পারে না।
জীবনে কিছু বিপ্লব আসে সরবে, ঢাকডোল পিটাইয়া। কিছু আসে নিঃশব্দে, মসৃণ সঞ্চারে, কিন্তু সমস্ত জীবনে এক ব্যাপক, সার্বিক পটপরিবর্তন ঘটাইয়া দেয়। তুলির সহিত বিবাহ কাজলের জীবনে সেই আশ্চর্য রূপান্তর লইয়া আসিল। প্রেম মানে যে কেবল শরীর নয়, বিবাহ মানেই কেবল শয্যা নয়, সেকথা কাজল জানিত। কিন্তু একটি তরুণী, সুন্দরী, মৃদু নারীর সান্নিধ্য মানুষকে যে কী স্বর্গের সন্ধান দিতে পারে তাহা সে এবার বুঝিল।
হৈমন্তীকে কিন্তু সত্যিই অনেকটা ছাড়িতে হইল। আগে নিজের লেখা ও পড়ার সময় বাদ দিয়া বাকি অবসরের সবটুকুই কাজল মাকে দিত। এখন হৈমন্তীর নিঃসঙ্গতা বাড়িয়া উঠিল। এক-একদিন ভুলিয়া ছেলের সঙ্গে কথা বলিবার জন্য দরজা পর্যন্ত গিয়া হৈমন্তী ফিরিয়া আসিয়াছে। ভিতরে পুত্রবধূর সঙ্গে ছেলে গল্প করিতেছে। কিছুই না, ব্যবধান কেবল একটি ভেজানো দরজা অথবা টানিয়া দেওয়া পর্দার, কিন্তু একদিন যেখানে অসংকোচ বিচরণের অধিকার ছিল, এখন সেখানে স্বপ্রযুক্ত বিচ্ছেদেব প্রান্তর।
হৈমন্তী ঘরে ফিরিয়া আসিয়া একটা বই খুলিয়া বসে।
তাহার আছে বই, আছে অপুর স্মৃতি, আছে জানালার বাহিরে রুদ্রপলাশ গাছে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত পাখি আর কাঠবেড়ালির খেলা, দিনের বিভিন্ন সময়ে আকাশের রঙ বদলানো। বয়েস বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে এইসব জিনিসকে হৈমন্তী অপরিবর্তনীয় এবং প্রকৃত সত্যের প্রকাশ হিসাবে নিজের জীবনে লাভ করিয়াছে।
এই অবস্থার অবসান ঘটিল আপনিই।
একদিন দুপুরের পর আকাশ কালো করিয়া মেঘ ঘনাইয়া আসিল। নিবিড় মেঘের ছায়ায় পৃথিবী মেদুর জলভরা ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে শুরু করিযাছে, বৃষ্টি নামিল বলিয়া। পুরোনো দিনের অভ্যাসমত হৈমন্তী ডাকিয়া উঠিল-ওরে খোন, দেখে যা কেমন সুন্দর মেঘ করেছে!
ডাক শুনিয়া ছেলের আগে ঘরে ঢুকিল তুলি। পেছন পেছন কাজল।
হৈমন্তীর একেবারে কোল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া তুলি বলিল—তাই তো মা, কী সুন্দর দেখাচ্ছে! তোমার ঘরের জানালা দিয়ে বেশি ভালো করে দেখা যায়। এদিকে একটু সরে যাও, আমরা তোমার কাছে বসি। আচ্ছা মা, নিশ্চিন্দিপুরে বা মৌপাহাড়িতে থাকার সময় এমন দিনে বাবা আর তুমি কী করতে বলল না—
তৃপ্তিতে হৈমন্তীর মন ভরিয়া গেল। সে বলিল—এরকম মেঘ দেখলেই তোমার শ্বশুরমশাই বলতেন-দ্যাখো দ্যাখো, কাকের ডিমের মতো মেঘ করেছে–
তুলি জিজ্ঞাসা করিল–কাকের ডিমের মতো মানে?
হৈমন্তী সস্নেহে বলিল—তুমি দেখ নি কখনও, না? কাকের ডিম কালোরঙের হয়। মেঘ ঘনিয়ে আসছে দেখলেই আমরা বেরিয়ে পড়তাম বেড়াতে–
–বৃষ্টি এলে ভিজতে না?
–ভিজতাম তো! হয়তো কুঠির মাঠ কিংবা কাচিকাটার পুলের কাছে চলে গিয়েছি, এমন সময় ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি নামতো। সেখানে আর কোথায় আশ্রয়? একটা গাছতলায় দাঁড়ালাম হয়তো, তা একটু পরে পাতা ফুড়ে সেখানেও জল পড়তে শুরু করল। তখন আবার হাঁটতে শুরু করতাম, দাঁড়িয়ে ভেজার চেয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভেজা আনন্দের। তোমার শ্বশুরমশাই গলা ছেড়ে গান গাইতে শুরু করে দিতেন, আমিও গাইতাম–
তুলি বলিল—বাবার গানের গলা খুব সুন্দর ছিল, না মা?
—হ্যাঁ বৌমা। তোমার শ্বশুরবংশে সবাই কিছু কিছু গাইতে পারে, তোমার বাবা খুব ভালো গাইতেন। দরাজ গলা ছিল। সুরের বোধ ছিল। নদীতে স্নান করবার সময় বিশুদ্ধ সংস্কৃতে শ্লোক উচ্চারণ করতেন, স্তবগান করতেন। সে সব গান আবার আমাকে শেখাতেন—
তুলি আরদারের সুরে বলিল—সে গান একটা শোনাও না মা—
লজ্জিতমুখে হৈমন্তী বলিল–না, সে কি আর এখন পারি বৌমা? সে থাক–
–না মা, একটা গান গাইতেই হবে, আমি তুলে নেব তোমার কাছ থেকে।
নদীতে স্নান করিবার সময় আরক্ষ জলে দাঁড়াইয়া অপু যে সংস্কৃত মন্ত্রটি গাহিত হৈমন্তী সেটি শুনাইল। তাহার গলা এখনও বেশ ভালো আছে, উচ্চারণও সুন্দর।
কয়েকদিন পরে কাজল অবাক হইয়া শুনিল তুলি ঘরের কাজ করিতে করিতে গুনগুন করিয়া সেদিনের শেখা গানটি গাহিতেছে। সে বলিল—বাঃ, এর মধ্যে শিখে নিলে গানটা?
—হুঁ মাকে আবার গাইতে বললাম, দু-তিনবারে উঠে গেল—
–বেশ, ভালো। তুমি গান শিখবে তুলি? তোমার গলা তো খুব সুন্দর!
তুলি রাজি হইল। কাজল স্থানীয় এক প্রবীণ গায়ককে অনুরোধ কৰায় তিনি সপ্তাহে একদিন তুলিকে গান শিখাইয়া যাইতেন। গানের ব্যাপারে তুলির স্বাভাবিক দক্ষতা কিছুদিনের মধ্যেই প্রকাশ পাইল। সমস্তু গানই সে অনায়াস দক্ষতায় শিখিয়া ফেলিত। শিক্ষক ভদ্রলোক একদিন কাজলকে বলিলেন—বৌমার সুরের বোধ খুব উঁচুদরের। অনেকদিন ধরে গান শেখাচ্ছি, এমনটি কমই দেখেছি। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত কিংবা টপ্পা অঙ্গের গান বৌমার গলায় খুব ভালো আসে। ওসব কঠিন গান সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী শিখতে চায় না, তারা চায় হালকা বাজার-চলতি গান চটপট তুলে নিতে। বৌমাকে শিখিয়ে আমার গান সার্থক হল–
কোন-কোনদিন খুব ভোরে উঠিয়া কাজল মা আর স্ত্রীকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হয়। ঘাসের ওপর তখনও শিশির শুকায় নাই, সূর্য উঠি উঠি করিতেছে। বাতাসে সকালের পবিত্রতা, কতরকম পাখি ডাকিতেছে গাছে গাছে। শহর হইতে বাহির হইয়া যে রাস্তাটা নদীর ধারে গিয়াছে তাহার দুধারে তেঁতুল, মেহগনি, শিরীষ, বকাইন আর কাঠবাদাম গাছ। মাঝে মাঝে দুয়েকটা জারুল বা ছাতিম। পথের ধারেই ঘন ঝোপঝাড়। এধারে বিশেষ বসতি গড়িয়া ওঠে নাই-শান্ত, স্নিগ্ধ বাতাস গায়ে মাখিয়া গল্প করিতে করিতে বেড়াইবার কী আনন্দ।
কঠ-র-র-র শব্দে কী একটা পাখি ডাকিয়া উঠিল। হৈমন্তী তুলির দিকে তাকাইয়া বলিল— শুনলে বৌমা?
–হ্যাঁ মা, কী পাখি ওটা?
–বলল তো কী?
তুলি চুপ করিয়া একটু ভাবিয়া বলিল–জানি না। তুমি বলে দাও—
হৈমন্তী হাসিয়া বলিল–ও হচ্ছে কাঠঠোকরা। ওটা ঠিক ডাক নয়, গাছের ডালে ঠোঁট ঠুকে ওইরকম আওয়াজ করে। ডাক অন্যরকম, শুনিয়ে দেবখন যদি ডাকে—
একটু একটু করিয়া তুলির জীবন সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেল। ইহার পূর্বে সে বিশেষ বাড়ির বাহিরে পা দেয় নাই, প্রকৃতির সহজ মজাগুলির সঙ্গে পরিচিত করাইয়া দিবার কেহ ছিল না। এখন শাশুড়ি ও স্বামীর মধ্যে দুইজন পরম সহানুভূতিশীল শিক্ষক পাইয়া তাহার জীবনের প্রকৃত শিক্ষা সবেগে অগ্রসর হইল। হৈমন্তী ঠিক সাধারণ মাপের নারী নহে, অপুর সঙ্গে অতিবাহিত জীবন তাহার অন্তরের সুর অনেক চড়া পর্দায় উঠাইয়া দিয়াছিল। পুত্রবধূকে হৈমন্তী সেই শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে লাগিল।
কাজল বাবার ডায়েরিতে তাহার শাশুড়ি লীলার কথা পড়িয়াছে, কিন্তু কখনও তাহার ছবি দেখে নাই। বিবাহের পর সে বিমলেন্দুর কাছ হইতে চাহিয়া লীলার একখানা ছবি জোগাড় করিয়াছে এবং ছবিখানা অ্যালবামে অপর্ণার ফোটোগ্রাফের পাশে লাগাইয়াছে। মাঝে মাঝে সে একান্ত মুহূর্তে ছবি দুটি দেখে।
হ্যাঁ, বাবা অথবা অন্যেরা মিথ্যা বলে নাই, তাহার শাশুড়ি দেখিতে সুন্দরী ছিলেন। দক্ষ শিল্পীর হাতে গড়া মূর্তির মতো অপার্থিব, অলৌকিক সৌন্দর্য পৃথিবীর পথেঘাটে এমন দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু–
কিন্তু তাহার মা যেন আরও সুন্দর।
পাতাকাটা চুল, পানের পাতার মতো মুখের গড়ন। ঠোঁটের সুকুমার ভঙ্গি তাহার মায়ের চেহারায় এক আশ্চর্য দেবীত্ব দান করিযাছে। কাহারও সঙ্গে তুলনা হয় না।
নাঃ, এসব ছেলেমানুষি দুজনেই মা, মায়েব রূপের তুলনা চলে না।
এইসময় হঠাৎ কাজলের কবিতা লিখিবাব ঝোঁক বাড়িয়া উঠিল। তুলির উদ্দেশে কবিতা লিখিয়া স্লিপগুলি ভাঁজ করিয়া বালিশের নিচে, টেবিলক্লথেব তলায় কিংবা তুলি যে বইখানা পড়িতেছে তাহার ফাঁকে রাখিয়া দিত। কবিতাগুলিকে বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য রতন হিসাবে উল্লেখ করা হয়তো একান্তই বাড়াবাড়ি হইবে, কিন্তু তুলি সেগুলি পাইযা ভারি খুশি হইত। ক্রমে ঘবের সমস্ত সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য স্থান কিছুক্ষণ বাদে খুঁজিযা দেখা তুলির অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গেল। কবিতা না পাইলে তাহার অভিমান হইত, মুখ গম্ভীর হইত। নিজের সৃষ্ট বিপদে কাজল আরক্ষ ডুবিয়া গেল। তুলির মুখ ম্লান হইলে তাহার জগৎ অন্ধকার হইয়া যায়, কিন্তু পত্নীকে প্রফুল্ল রাখিবার জন্য প্রতিদিন ডজনখানেক কবিতা স্বয়ং মহাকবি কালিদাসও লিখিতে পারিতেন কি? প্রাণের দায়ে কাজল এই অসম্ভব কাজেও প্রায় অভ্যস্ত হইয়া আসিল।
এক ছুটির দুপুরে সদ্য আবিষ্কৃত গোটাদুই কবিতা পাঠান্তে তুলি বলিল—বেশ হয়েছে, তোমার কবিতার হাত বেশ ভালো। আমি একটাও হারাই নি, জানো তো? সবগুলো একজায়গায় করে বাক্সে রেখে দিয়েছি। এই এত মোটা হয়েছে। আচ্ছা, তুমি ছবি আঁকতে পারো না? কবিতার সঙ্গে ছবি থাকলে দেখতে কত ভালো লাগে–
প্রিয়ার অনুরোধ রক্ষার জন্য যুগে যুগে মানুষ রাক্ষস-রক্ষিত সরোবর হইতে সোনার পদ্ম তুলিতে গিয়াছে, প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধ করিয়াছে, স্বর্ণমৃগের সন্ধানে গহন বনে ফিরিয়াছে, ছবি আঁকা আর এমন কী কাজ?
কাজল চিত্রশিল্পীতে পরিণত হইল।
সাধনার পথে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া কাজল বুঝিল বিপদ এইবার গভীরতর। কিছুটা সাহিত্যপ্রতিভা থাকিলে যা হোক করিয়া একটা কবিতা দাঁড় করাইয়া দেওয়া যায়, বিশেষ করিয়া যে কবিতা মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা করিয়া পড়া হইবে না, বস্তুত মাত্র একজন ব্যতীত সমস্ত পৃথিবীতে যে কবিতার আর পাঠকই নাই। কিন্তু ছবি আঁকিতে গেলে কিঞ্চিৎ বেশি দক্ষতা ও স্বভাবনৈপুণ্যের প্রয়োজন হয়। কাজে নামিয়া কাজল বুঝিল এ কাজ তাহার নয়। পাখি আঁকিলে বিকলাঙ্গ জিরাফের ছানার মতো দেখায়, মেঘের আড়াল হইতে সূর্যরশ্মি বাহির হইতেছে আঁকিলে মনে হয় বড়ো একতাল ময়দার মধ্যে কয়েকটা সরু কাঠি গোঁজা আছে। একবার তুলির মুখখানিকে পদ্মের সঙ্গে তুলনা করিয়া পুকুরে অনেক পদ্মপাতার মধ্যে একখানি ফুল ফুটিয়া আছে এমন একটি ছবি আঁকিতে চেষ্টা করিল। আঁকা শেষ হইলে মনে হইল জলে অনেকগুলি তেলেভাজা মশলাপাপড় ভাসিয়া আছে, তাহার মাঝখানে একটা জটিল কী যেন—আর যা হউক, সেটি পদ্ম নয়।
প্রায় হতাশ হইয়া পড়িবার মুখে আশার আলো দেখা দিল।
কাজল আবিষ্কার করিল সে খুব সহজেই বেড়াল আঁকিতে পারে। সেগুলি যে অবিকল বেড়াল হয় এমন নয়, কিন্তু সাদৃশ্যের যাবতীয় গুরুতর অসঙ্গতি সত্ত্বেও তাহাদের চিনিতে ভুল হয় না। তুলির স্বভাব, চেহারা ইত্যাদির সঙ্গে বেড়ালছানার তুলনা করিয়া কাজল একখানি দুইপাতাব্যাপী কবিতা লিখিল এবং স্থানে স্থানে গোটাকতক মার্জারশাবকের বিভিন্ন ভঙ্গিমার ছবি আঁকিয়া বসাইয়া দিল। একরঙা ছবিতে মজা নাই, তাই রঙপেন্সিল দিয়া ছবিগুলিকে মনোহারী রঙে রঞ্জিত করিল। নেহাত প্রেম যৌক্তিকতার ধার ধারে না তাই রক্ষা, নহিলে নীল, সবুজ আর ম্যাজেন্টা রঙের চৌখুপিওয়ালা শতরঞ্চির ডিজাইনের বেড়াল দেখিলে স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টাও চমকাইয়া উঠিতেন।
যাহার জন্য ছবি সে কিন্তু খুব খুশি হইল।
কবিতা পড়া হইলে ছবিগুলি ভালো করিয়া আবার দেখিতে দেখিতে উজ্জ্বলমুখে তুলি বলিল—তুমি ছবিও আঁকতে পারা কখনও বলল নি তো! চমৎকার বেড়াল, বেশ বেড়াল।
কাজল বলিল–বেড়ালছানাগুলো কিন্তু তোমাকে ভেবে আঁকা–
—আমাকে? কেন?
—তুমিও ওইরকম নরম নবম, তুলতুলে—
তুলি লজ্জা পাইল, বলিল—যাঃ, যতসব বাজে কথা—
তাহার পর কী ভাবিয়া বলিল—তা হোক, তুমি কবিতার সঙ্গে বেড়াল এঁকো।
অতঃপর কাব্য ও শিল্পচর্চা সমান্তরালভাবে সমানবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল।
কাজল চিরকালের অভ্যাসমত অনেকরাত অবধি পড়াশুনা করে। এক-একদিন বই হইতে চোখ সরাইয়া দেখিত তুলি তাহার পাশে পরম নির্ভরতায় ঘুমাইয়া আছে। রবীন্দ্রনাথ নৌকাডুবিতে যেমন লিখিয়াছেন, তাহার মুখখানি যেন তেমনই সমস্ত বিশ্বচবাচরে একটিমাত্র দেখিবার জিনিসের মতো ফুটিযা আছে। তুলিব ঘুমন্ত মুখে গার্হস্থ্য শান্তি আলো।
মনে কেমন একটা আনন্দ। দুর্লভ বস্তু একান্তভাবে লাভ করিবার আনন্দ।
সরল পৃথিবীর যে স্বপ্নের মধ্যে কাজলের বড়ো হইয়া ওঠা, তাহা একটু একটু করিয়া ভাঙিয়া যাইতেছিল। এবার একটি ঘটনায় সে বুঝিল মানুষের মুখ মোটেই তাহার মনের দর্পণ নয়। তিক্ততার মূল্যে সে কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিল।
একদিন সকালে নিশ্চিন্দিপুর হইতে একজন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। কাজলকে দেখিয়া সে বলিল—দাদাবাবু না? নমস্কার দাদাবাবু, ভালো আছেন? কাকীমা কই?
কাজল বলিল—তোমাকে তো ভাই চিনলাম না! কে তুমি?
–চিনবেন আর কী করে? দেশে যাতায়াত বড্ডই কমিয়ে দিয়েছেন কর্তামশাই থাকলে চিনতে পারতেন। আমার নাম শিবু রায়, আপনাদের গাঁয়েরই চড়কতলার মাঠের ধারে আমার বাড়ি। তা পরিচয় দেবার মতো কিছু নেইও, ব্রাহ্মণবংশে জন্ম—এইমাত্র। গরিব ঘরে জন্মেচি দাদাবাবু, পয়সার অভাবে লেখাপড়া শিখতে পারিনি, জন খেটে পেট চালাই। কাকীমাকে প্রণাম করতে ইচ্ছে হল, তাই চলে এলাম। ভোর রাত্তিরের ট্রেন ধরিচি–
হৈমন্তীকে প্রণাম করিয়া এবং স্বৰ্গত কর্তামশাইকে স্মরণ করিয়া শিবু কাঁদিয়া আকুল হইল, তুলিকে দেখিয়া বার বার মা যেন আমার সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী বলিল, এবং বাহিরের বারান্দায় বসিয়া পরোটা, আলুচচ্চড়ি ও আখের গুড় সহযোগে অবিশ্বাস্য-পরিমাণ জলখাবার খাইল। তাহার হাঁটু পর্যন্ত খাটো কাপড়, ছেঁড়া নীলরঙের হাতকাটা ময়লা হাফশার্ট ও বুভুক্ষু চেহারা দেখিয়া কাজলের মায়া হইল! আহা, বেচারা ভালো করিয়া খাইতে পায় না। তাহারই গ্রামের লোক, উহাকে আজ দুপুরে ভালো করিয়া খাওয়াইতে হইবে।
কাজল বলিল—তুমি খেয়েদেয়ে একেবারে ওবেলা যাবে কিন্তু। মাংস খাও তো?
শিবু রায় আকর্শ হাসিল।—আজ্ঞে, খাই বইকি। খুব ভালোবাসি। তবে পাচ্ছি কোথায়? আমরা গরিব-গুরবো লোক, মাংস কি কিনে খেতে পারি? আজ আপনার দয়ায়–
শিবুর উচ্ছাসকে বাড়িতে না দিয়া কাজল ব্যাগ হাতে বাজারে বাহিরে হইল।
দুপুরে খাইবার সময় বোঝা গেল সকালে শিবুর জলখাবার খাইবার যে বহর দেখিয়া কাজল বিস্মিত হইয়াছিল, সেটা শিবুর প্রকৃত আহারগ্রহণ ক্ষমতার সামান্য ভূমিকামাত্র। আর একটু হইলেই কাজলকে সে-বেলা সপরিবারে উপবাসে থাকিতে হইত।
বেলা তিনটা নাগাদ শিবু ফিরিবার ট্রেন ধরিবার জন্য তৈরি হইয়া হৈমন্তীকে বলিল—ভালো কথা কাকীমা, আপনাদের অনেক জমি তো গ্রামে এমনি পড়ে রয়েছে, কাউকে দিয়ে চাষ করান না কেন? গ্রামের ভেতরের জমিতে তৈরি তবি-তরকারি লাগালে ভালো ফসল পেতেন। ফেলে রেখে লাভ কী? কখন বেদখল হয়ে যায়—বুঝলেন না?
হৈমন্তী বলিল—ওসব ঝামেলা কে করে বাবা? আমার তেমন লোক কই?
শিবু হাতজোড় করিয়া বলল—কেন, আমিই তো আছি কাকীমা। আপনাদের পুরোনো ভিটের পাশ দিয়ে যদি এখন বেগুনের চারা বসানো যায় তাহলে এবাব শীতে বেগুন খেয়ে শেষ করতে পারবেন না। দিন দেখি আমায় পঞ্চাশটা টাকা, আমি ভুই তৈরি করে চারা বসিয়ে দেব। তদারকও আমিই করব। ফসল অর্ধেক আমার, অর্ধেক আপনার।
কথাটা হৈমন্তীর ভালো লাগিল। বেগুন এমন কিছু জিনিস নয়, কিন্তু নিজেদের জমিতে তাহা উৎপন্ন হইবে ভাবিলে আনন্দ হয়। টাকা দিলে গরিব লোকটারও কিছু উপকার করা হইবে। নিজ শ্রমের বিনিময়ে শিবু শীতকালে কিছু উপার্জন করিয়া লইতে পারিবে।
হৈমন্তী তাহার হাতে পঞ্চাশটা টাকা দিল।
পনেরো-কুড়িদিন বাদে বাদে শিবু আসিতে লাগিল। প্রথমবার আসিয়া সে বলিল–চারা লাগানো হয়ে গিয়েছে কাকীমা। অনেকদিন পড়ে থাকা ভুই, চারা লাগানোমাত্র চট করে ধরে নিয়েছে, একেবারে নতুন করে বাড়ছে। তা গোটাকুড়ি টাকা যদি দেন তো বড়ো ভালো হয়, পাহারা দেবার জন্য একটা ছোঁড়াকে লাগাবো। এই বয়েসে রাত জাগতে পাবিনে আর–
টাকা পাইয়া সে চলিয়া গেল।
দিনকুড়ি বাদে আবার আসিয়া হাজির। হৈমন্তী বলিল—কী বাবা, জমির খবর কী?
-ওঃ, খুব ভালো কাকীমা। গাছে বেগুন ধরেছে। দেখবেন এখন এক-একখানা কেমন নিকাটা মুক্তকেশী বেগুন হবে। ইয়ে হয়েছে, গোটা পঁচিশ টাকা যে দরকার—
–আবার টাকা কী হবে?
—নিড়েন দিতে হবে জমিতে। আগাছায় ভরে যাচ্ছে। একা কি আর পারি?
মোট টাকা যা গেল প্রাপ্ত ফসলের দামের সহিত তাহার সঙ্গতি থাকিবে না বলিয়াই মনে হইল। কিন্তু এখন আর থামা যায় না।
শীতের প্রায় মাঝামাঝি শিবু সের দুই মাঝারি আকারের বেগুন গামছায় বাঁধিয়া আনিল।
–কাকীমা, নিন জমির বেগুন। খেয়ে দেখবেন কেমন স্বাদ।
ফসল তুলিবার খরচ বাবদ কুড়ি টাকা লইয়া সে বিদায় হইল।
হৈমন্তী জমির প্রথম ফসল পাইয়া ভারি খুশি। ভাগ্যিস শিবু ছিল।
কিন্তু শিবু আর আসিল না। ফসলের আকাঙ্ক্ষিত বাকি বস্তাও আসিয়া পৌঁছাইল না। খবর লইয়া জানা গেল পুরোনো ভিটের জমিতে একটিও বেগুনচারা বসে নাই। শিবু ওই দুই সের বেগুন আষাঢুর হাট হইতে কিনিয়া আনিয়াছিল। বর্তমানে সে চুরি করিয়া জেলে আছে।
কাজলদের পারিবারিক কৃষি-উদ্যোগ সে বৎসর বেগুনের মরশুমের সঙ্গেই শেষ হইয়া গেল।