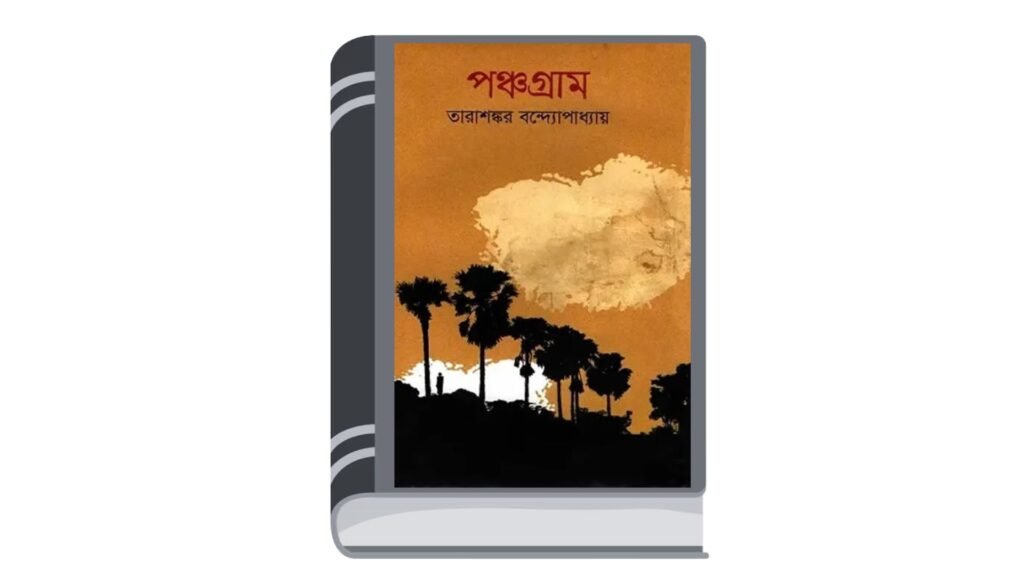১৯. দুইটা ঘটনা ঘটিয়া গেল
পনের দিনের মধ্যেই এ অঞ্চলে বেশ একটা সাড়া পড়িয়া গেল। দুইটা ঘটনা ঘটিয়া গেল। শ্ৰীহরি ঘোষ পঞ্চায়েত ডাকিয়া দেবুকে পতিত করিল। অন্যদিকে বন্যা-সাহায্য-সমিতি বেশ একটি চেহারা লইয়া গড়িয়া উঠিল। সাহায্য-সমিতির জন্যই অঞ্চলটায় বেশি সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। ঠাকুর মহাশয়ের নাতি বিশ্বনাথবাবু নাকি গেজেটে বানের খবর ছাপাইয়া দিয়াছেন। কলিকাতা, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা প্রভৃতি বড় বড় শহর হইতে চাঁদা তুলিতেছেন; শুধু শহর নয়, অনেক পল্লীগ্রাম হইতেও লোক টাকা পাঠাইতেছে। প্রায় নিত্যই দেবু পণ্ডিতের নামে কত নাম-না–জানা গ্রাম হইতে পাঁচ টাকা দশ টাকার মনিঅৰ্ডার আসিতেছে। পনের-কুড়ি দিনের মধ্যেই প্রায় পাঁচশ টাকা দেবুর হাতে আসিয়াছে। যাহাদের ঘর ভাঙিয়াছে, তাহাদের ঘরের জন্য সাহায্য দেওয়া হইবে। বীজধান ইতিমধ্যেই দেওয়া হইয়া গিয়াছে। মাঠে আছাড়োর বীজচারা হইতে যে যেমন পারিয়াছে—সে তেমন জমি আবাদ করিতেছে।
ভাদ্রের সংক্রান্তি চলিয়া গেল; আজ আশ্বিনের পয়লা। আশ্বিনের রোপণ কিস্কে? অর্থাৎ কিসের জন্য। তবু লোকে এখনও রোয়ার কাজ চালাইতেছে। মাসের প্রথম পাঁচটা দিন গতমাসের শামিল বলিয়াই ধরা হয়। তাহার উপর এবার ভাদ্র মাসের একটা দিন কমিয়া গিয়াছেঊনত্রিশ দিনে মাস ছিল। তবে বিপদ হইয়াছে—লোকের ঘরে খাবার নাই, তাহার উপর আরম্ভ হইয়াছে কম্প দিয়া জ্বর ম্যালেরিয়া। ভাগ্য তবু ভাল বলিতে হইবে যে কলেরা হয় নাই। ঘরে ঘরে শিউলিপাতার রস খাওয়ার এক নূতন কাজ বাড়িয়াছে। ভদ্রের শেষে শিউলিগাছগুলা নূতন পাতায় ভরিয়া ওঠে, ফুল দেখা দেয়; এবার গাছের পাতা নিঃশেষ হইয়া গেল-এ বৎসর গাছগুলার ফুল হইবে না। জ্বর আরম্ভ না হইলে আরও কিছু বেশি জমি আবাদ করা যাইত। কাল ম্যালেরিয়া! ম্যালেরিয়া প্রতি বৎসরেই এই সময়টায় কিছু কিছু হয়, এবার এই বানের পর ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছে ভীষণভাবে! ওষুধ বিনা পয়সায় পাওয়া যায় কঙ্কণার ডাক্তারখানায় আর জংশন শহরের হাসপাতালে; কিন্তু চাষ কামাই করিয়া এতটা পথ রোগী লইয়া যাওয়া সহজ কথা নয়। জগন ডাক্তার বিনা পয়সায় দেখে, কিন্তু ওষুধের দাম নেয়। না লইলেই বা তাহার চলে কি করিয়া? তবে দেবু পণ্ডিত কাল বলিয়াছে-কলিকাতা হইতে কুইনাইন এবং অন্যান্য ওষুধ আসিতেছে। জেলাতেও নাকি দরখাস্ত দেওয়া হইয়াছে—একজন ডাক্তার এবং ওষুধের জন্য।
লোকের বিস্ময়ের আর অবধি নাই। বুড়ো হরিশ সেদিন ভবেশকে বলিল—যা দেখি নাই বাবার কালে, তাই দেখালে ছেলের পালে।
ভবেশ বলিল–তা বটে হরিশ-খুড়ো। দেখলাম অনেক। বান তো আগেও হয়েছে গো। …
নদীমাতৃক বাংলাদেশ। বর্ষা এখানে প্রবল ঋতু। জল-প্লাবন অল্পবিস্ত প্রতি বৎসরই হইয়া থাকে। পাহাড়িয়া নদী ময়ূরাক্ষীর বুকেও বিশ-ত্রিশ বৎসর অন্তর প্রবল বর্ষয় এইভাবেই সর্বনাশা রাক্ষসী বন্যার ঢল্ নামে; গ্রাম ভাসিয়া যায়, শস্যক্ষেত্র ড়ুবিয়া যায়—এ তাহারা বরাবরই দেখিয়া আসিতেছে। তখনকার আমলে এমন বন্যার পর দেশে একট দুঃসময় আসিত। সে দুঃসময়ে স্থানীয় ধনী এবং জমিদারেরা সাহায্য করিতেন। ধনীরা, অব ছাপন্ন গৃহস্থেরা গরিবদের খাইতে দিত; মহাজনেরা বিনা-সুদে বা অল্প-সুদে ধান-ঋণ দিত চাষীদের। জমিদার সে সময় আশ্বিনকিস্তির খাজনা আদায় বন্ধ রাখিত, সে-বৎসরের খাজনা বাকি পড়িলে সুদ লইত না। দয়ালু জমিদার আংশিকভাবে খাজনা মাফ দিত, আবার দুই-একজন গোটা বৎসরটাই খাজনা রেয়াত করিত। চাষীদের অবস্থা তখন অবশ্য এখনকার চেয়ে অনেক ভাল ছিল, এমন করিয়া সম্পত্তিগুলো টুকরা টুকরা হইয়া গৃহস্থেরা গরিব হইয়া যায় নাই। তাহারা কয়টা মাস কষ্ট করিত, তাহার পর আবার ধীরে ধীরে সামলাইয়া উঠিত।
গরিব-দুঃখী অর্থাৎ বাউরি-ডাম-মুচিদের দুর্দশা তখনও যেমন, এখনও তেমনই। এই ধরনের বিপর্যয়ের পর তাদের মধ্যেই মড়ক হয় বেশি। ভিক্ষা ছাড়া গতি থাকে না, দলে দলে গ্রাম ছাড়িয়া গ্রামান্তরে চলিয়া যায়। আবার দেশের অবস্থা ফিরিলে পিতৃপুরুষের ভিটার মমতায় অনেকেই ফেরে। এমন দুর্দশায় সম্পন্ন গৃহস্থেরা গভর্নমেন্টের কাছে দরখাস্ত করিয়া তাকাবি ঋণ লইত, পুকুর কাটাইত, জমি কাটাইত, গরিবরা তাহাতে খাঁটিয়া খাইত।
হরিশ বলিল-ওদের কাল তো এখন ভাল হে। নদীর পুল পার হলেই ওপারে জংশন। বিশটা কলে ধোঁয়া উঠছে। গেলেই খাটুনি সঙ্গে সঙ্গে পয়সা। তা তো বেটারা যাবে না।
ভবেশ বলিল—যায় নাই তাই রক্ষে খুড়ো! গেলে আর মুনিষ-বাগাল মিলত না।
হরিশ বলিল—তো বটে। তবে এবারে আর থাকবে না বাবা। এবার যাবে সব। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা।
ভবেশ বলিল—দেবু তা লেগেছে খুব। ইস্কুলের ছোঁড়ারা সব গায়ে-গায়ে গান গেয়ে ভিক্ষে করছে। চাল, কাপড়, পয়সা।
গৌর দেবুকে যে কথাটা কানে কানে বলিয়াছিল, সে কথাটা কাজে পরিণত হইয়াছে। এক-একজন বয়স্ক লোকের নিয়ন্ত্রণে ছেলের দল যেসব গ্রামে বন্যা হয় নাই সেই সব গ্রাম ঘুরিয়া, গান গাহিয়া, চাল, কাপড় ভিক্ষা করিয়া আনিতেছে। পনের কুড়ি মন চাউল ইহার মধ্যে জমা হইয়াছে। কোনো এক ভদ্রলোকের গ্রামে মেয়েরা নাকি গয়না খুলিয়া দিয়াছে। খুব দামি গয়না নয়; আংটি, দুল, নাকছবি ইত্যাদি। এসবই এই অঞ্চলের লোকের কাছে অদ্ভুত ঠেকিতেছে। লোকের বাড়িতে গরিবেরা নিজে যখন ভিক্ষা চাহিতে যায়, তখন লোকে দেয় না, কটু কথা বলে। কত কাতরভাবে কাকুতি মিনতি করিয়া তাহাদের ভিক্ষা চাহিতে হয়। অথচ এই ভিক্ষার মধ্যেওই ভিক্ষার দীনতা নাই। আবার দেবুর বাড়িতে সাহায্য যাহারা লইতেছে, তাহাদের গায়েও ভিক্ষার দীনতার অ্যাঁচ লাগিতেছে না। সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে একটা অপূর্ব আত্মতৃপ্তির ভাব যেন লুকানো আছে। আগে নিঃস্ব রিক্ত মানুষগুলি দারিদ্র্যের জন্য ভিক্ষা করিতে গিয়া একটা মর্মান্তিক অপরাধবোধের গ্লানি অনুভব করিত; সেই অপরাধবোধটা যেন ঘুচিয়া গিয়াছে।
ভবেশ বলিল—বেজায় বড় কিন্তু বেড়ে গেল ছোটলোকের দল। ওই সাহায্য-সমিতির চাল পেয়ে বেটাদের বৃদ্ধি হয়েছে দেখেছ? পরশু আমাদের মান্দের (বড় রাখাল) ছোঁড়া একবেলা এল না। তা গেলাম পাড়াতে। ভাবলাম অসুখবিসুখ হয়েছে, গিয়ে শুনলাম তিনকড়ির বেটা গৌরের সঙ্গে জংশনে গিয়েছে—কি কাজ আছে। আমার রাগ হয়ে গেল। রাগ হয় কিনা তুমিই বল? বললাম তা হলে কাজকর্ম করে আর কাজ নাই-আমি জবাব দিলাম। ছোঁড়ার মা বললে কি জান? বললে—তা মশায় কি করব বল? পণ্ডিত মাশায়রা খেতে দিচ্ছে লোককে এই বিপদে। তাদের একটা কাজ না করে দিলে কি চলে? যদি জবাবই দাও তো দিয়ে।
হরিশ হাসিয়া বলিল–ও হয়। চিরকালই ওই হয়ে আসছে। বুঝলে—আমরা তখন ছোট, এই ভের-চৌদ্দ বছর বয়সে। তখন রামদাস গোঁসাই এসেছিল। নাম শুনেছ তো?
ভবেশ প্রণাম করিয়া বলিল-ওরে বারে! আমি দেখেছি যে!
হরিশ বলিল—দেখেছ?
–হ্যাঁ, ইয়া জটা। দেখি নাই! তখন অবিশ্যি আর এখানে থাকেন না। মধ্যে মধ্যে আসতেন।
—তাই বল। আমি যখনকার কথা বলছি, গোঁসাই বাবা তখন এখানেই থাকতেন। কঙ্কণার উদিকের মাথায় ময়ূরাক্ষীর ধারে তার আস্তানা। গোঁসাই লাগিয়ে দিলেন মদ্বের ধুম। লোকে নিজেরা মাথায় করে দুমন-দশমন চাল দিয়ে আসত। গরিব-দুঃখী যে যত পারত খেতে পেত, কেবল মুখে বলতে হত বলো ভাই রাম নাম, সীতারাম। গরিব-দুঃখীর মা বাপ ছিলেন গোঁসাই। তখন এমনই বাড় হয়েছিল ছোটলোকের জমিদার, গেরস্ত একটা কথা বললেই বেটারা গিয়ে দশখানা করে লাগাত গোঁসাইয়ের কাছে। গোঁসাইও সেই নিয়ে জমিদার গেরস্তদের সঙ্গে ঝগড়া করতেন। শেষকালে লাগল কঙ্কণার বাবুদের সঙ্গে। তা গোঁসাই লড়েছিলেন অনেকদিন। শেষকালে একদিন এক খেমটাওয়ালী এসে হাজির হল। বাবুদের চক্রান্ত, বুঝলে? গোসাইকে ধরে বললেশহরে গিয়ে তুমি আমার ঘরে ছিলে, টাকা বাকি আছে, টাকা দাও। নইলে …।এই নিয়ে সে এক মহা কেলেঙ্কারি। গোঁসাই রেগেমেগে চলে গেলেন, বলে গেলেন-কল্কিমহারাজ না এলে দুষ্টের দমন হবে না। … ব্যস, তারপর আবার যে কে। সেই—সেই পায়ের তলায়! এও দেখো তাই হবে।
সেকালে রামদাস গোঁসাইয়ের কাছে ওই রূপ-পসারিনী আসিতেই লোকে গোঁসাইকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। পর পর তিন-চারিদিন তৈয়ারী ভাত-তরকারি নষ্ট হইয়া গেল, কেহ আসিল না। যাহাদের হইয়া গোসাই জমিদারের সঙ্গে বিবাদ করিয়াছিলেন—তাহারাও আসে নাই, রামদাস গোঁসাই রোষে ক্ষোভে এ স্থান ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। একালে কিন্তু একটা পরিবর্তন দেখা গিয়াছে। দেবুর সঙ্গে কামার-বউ এবং দুর্গাকে জড়াইয়া অপবাদটা লইয়া আলোচনা লোকে যথেষ্ট করিয়াছে, পঞ্চায়েত দেবুকে পতিত করিয়াছে; তবু লোকে তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই।
দেবুর প্রতি ন্যায়রত্নের বিশ্বাস অগাধ। কিন্তু জনসাধারণকে তিনি সে বিশ্বাস করেন না; এই বিষয়টা লইয়া তিনিও ভাবিয়াছেন। তাহার এক সময় মনে হয় সমাজ-শৃঙ্খলা ভাঙিয়া টুকরা। টুকরা হইয়া গিয়াছে, সমাজ ভাঙিবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ধর্মবিশ্বাসও লোপ পাইতে বসিয়াছে। সেইজন্য নবশাক সম্প্রদায়ের পঞ্চায়েত শ্ৰীহরি ঘোষের নেতৃত্বে থাকিয়া দবুকে পতিত করিবার সংকল্প করিলেও সেটা ঠিক কাজে পরিণত হইল না। ইহারই মধ্যে একদিন শিবকালীপুরের চণ্ডীমণ্ডপে বর্তমানে শ্ৰীহরি ঘোষের ঠাকুরবাড়িতে-ঘোষের আহ্বানে নবশাক সম্প্রদায়ের পঞ্চায়েত সমবেত হইয়াছিল। স্থানীয় অবস্থাপন্ন সৎগৃহস্থ যাহারা, তাহাদের অনেকেই আসিয়াছিল। গরিবেরাও একেবারে না-আসা হয় নাই। দেবুকে ডাকা হইয়াছিল কিন্তু সে আসে নাই। বলিয়া দিয়াছিল—কামার-বউ শ্ৰীহরি ঘোষের বাড়িতে আছে; পূর্বে সে তাহাকে সাহায্য করিত নিরাশ্রয় বন্ধুপত্নী হিসাবে, কিন্তু এখন তাহার সঙ্গে তাহার কোনো সম্বন্ধই নাই। দুর্গা তাহাকে শ্রদ্ধাভক্তি করে। দুর্গার মামার বাড়ি তাহার শ্বশুরের গ্রামে, সেই হিসাবে দুর্গা তাহার স্ত্রীকে দিদি বলিত, তাহাকে জামাই-পণ্ডিত বলে। সে দুর্গাকে স্নেহ করে। দুর্গা তাহার বাড়িতে কাজকর্ম করে এবং বরাবরই করিবে; সেও তাহাকে চিরদিন স্নেহ এবং সাহায্য করিবে; কোনো দিন তাড়াইয়া দিবে না। এই তাহার উত্তর। এই শুনিয়া পঞ্চায়েত যাহা খুশি হয় করিবেন।
পঞ্চায়েত তাহাকে পতিত করিয়াছে।
পতিত করিলেও জনসাধারণ দেবুর সংস্রব ত্যাগ করে নাই। লোকে আসে যায়, দেবুর। ওখানে বসে, পান-তামাক খায়। বিশেষ করিয়া সাহায্য-সমিতি লইয়া দেবুর সঙ্গে তাহাদের। ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা। আবার সাধারণ অবস্থার লোকেদের মধ্যে কতকগুলি লোক তো পঞ্চায়েতের ঘোষণাকে প্রকাশ্যেই মানি না বলিয়া দিয়াছে। তিনকড়ি তাহাদের নেতা।
ন্যায়রত্ন যেদিন দেবুকে উপদেশ দিয়াছিলেন—সেদিন কল্পনা করিয়াছিলেন অন্যরূপ; কল্পনা করিয়াছিলেন সমাজের সঙ্গে কঠিন বিরোধিতার মধ্যে পণ্ডিতের ধৰ্মজীবন উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। ধ্যান-ধারণা পূজার্চনার মধ্য দিয়া দেবুর এক নূতন রূপ তিনি কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে কল্পনা ব্যর্থ হইয়াছে। দেবু ঘোষ সাহায্য-সমিতি লইয়া কর্মের পথে চলিয়াছে। কর্মের পথেও ধর্ম জীবনে যাওয়া যায়। কিন্তু দেবুর সম্বন্ধে একটা কথা শুনিয়া বড় আঘাত পাইয়াছেন। দেবু নাকি দুর্গা মুচিনীর হাতে জল খাইতেও প্রস্তুত। দুর্গাকে সে অনুরোধও করিয়াছিল; কিন্তু দুর্গা রাজি হয় নাই।
কর্মকেই তিনি সামাজিক জীবনের সঞ্জীবনীশক্তি বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সে কর্ম ধর্ম বিবর্জিত কর্ম নয়। ধর্ম-বিবর্জিত কর্ম সঞ্জীবনী সুধা নয়—উত্তেজক সুধা, অন্ন নয়—পচনশীল তণ্ডুলের মাদক রস।
ন্যায়রত্ন দেবুর জন্য চিন্তিত হইয়াছেন। পণ্ডিতকে তিনি ভালবাসেন। পণ্ডিত মাদক রসের উত্তেজনায় উগ্ৰ উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছে। এটা তিনি আগে কল্পনা করেন নাই। সমাজে এমনিভাবেই জোয়ার-ভাটা খেলিতেছে। এমনিভাবেই মানুষগুলি এক-একবার জোয়ারের উচ্ছ্বাস লইয়া উঠিতেছে, আবার সে উচ্ছাস ভাঙিয়া পড়িয়া ভাটার টানের মত শান্ত স্তিমিত হইয়া যাইতেছে।
এ তো ক্ষুদ্র পঞ্চগ্ৰাম। সমগ্র দেশ ব্যাপ্ত করিয়া এমনিভাবে উচ্ছাস আসে যায়। তাহার জীবনেই তিনি দেখিয়াছেন ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলন। অবশ্য ব্রাহ্মধর্মে সাধারণ মানুষের জীবন। একবিন্দুও আকৃষ্ট হয় নাই। তারপর আসিল স্বদেশী আন্দোলন; সে আন্দোলনেও দুইটি উচ্ছাস দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল। স্বদেশী আন্দোলনই—ধৰ্মসংস্রবহীন প্রথম আন্দোলন। এই আন্দোলন একটা কাজ করিয়াছে। না থাক ধর্মের সংস্রব, কিন্তু একটা নৈতিক প্রভাব আনিয়া দিয়া গিয়াছে।
তাহার প্রথম জীবনে তিনি যাহা দেখিয়াছেন সে দৃশ্য তাহার মনে পড়িল। প্রথম। সমাজপতির আসনে বসিয়া নিজে তিনি মর্মান্তিক বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন। নামে তিনি সমাজপতি হইলেও তখন হইতেই সত্যকার সমাজপতি ছিল জমিদার। জমিদারের তখন প্রবল। প্রতাপ। তাহারা তাহাকে মুখে সন্মান করিত, শ্ৰদ্ধা করিত; কিন্তু অন্তরে করিত উপেক্ষা। সাধারণ ব্যক্তিকে শাস্তি দিবার ক্ষেত্রে তাঁহাকে তাহারা আহ্বান করিত। কিন্তু নিজেদের ব্যভিচারের অন্ত ছিল না। মদ্যপান ছিল তন্ত্রশাস্ত্ৰ-অনুমোদিত; জমিদারের বৈঠকে বসিত কারণ চক্র। পথে পথে তরুণ ধনী-নন্দনেরা মত্ত পদবিক্ষেপে কদর্য ভাষায় গালিগালাজ করিয়া ফিরিত। রাত্রে অসহায় মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্রের দরজায় কামোন্মত্ত করাঘাত ধ্বনিত হইত। সাধারণ মানুষ ছিল বোব জানোয়ারের মত। তাহাদের ঘরের অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। এই স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ সেইটাকে অনেকটা ধুইয়া মুছিয়া দিয়া গিয়াছে; মানুষের একটা নীতিবোধ জাগিয়াছে।
ন্যায়রত্ন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। এই আন্দোলনের ঢেউ তাহার শশীর বুকে। লাগিয়াছিল। শশীর মধ্যে দুর্নীতি কিছু ছিল না। আন্দোলন তাহার ধর্মবিশ্বাস ক্ষুণ্ণ করিয়া দিয়াছিল। শশী উদ্ধত হইয়া উঠিয়ছিল। তাহার ফল ন্যায়রত্নের জীবনে ভীষণতম আকারে দেখা দিয়াছে। আবার সেই আন্দোলনের ঢেউ লাগিয়াছে বিশ্বনাথের বুকে। বিশ্বনাথ তাহার মুখের উপরেই বলিয়াছে—সে জাতি মানে না, ধৰ্ম মানে না, সমাজ ভাঙিতে চায়। সে তাহার বংশের উত্তরাধিকার পর্যন্ত অস্বীকার করিতে চায়। জয়ার মত স্ত্রী—তাহার প্রতিও তাহার মমতা নাই। এবারকার জোয়ার সর্বনাশা জোয়ার … আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন ন্যায়রত্ন।
পঞ্চগ্রামের বুকেও সেই জোয়ার-ভাটা চলিয়াছে। নানা ঘটনা উপলক্ষ করিয়া মানুষগুলি এক-এক সময় হইচই করিয়া কলরব করিয়া ওঠে, আবার এলাইয়া পড়ে-দল ভাঙিয়া যায়। আগে প্রতি হইচই-এর ভিতরেই থাকিত সমাজ-ধর্ম। তাহার প্রথম জীবনে হইচই হইয়াছিল–তাঁহারই নেতৃত্বে কঙ্কণার চণ্ডীতলায় বাবুদের যথেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদে। পাঁচখানা গ্রামের মেয়েরা সেখানে যায়, বাবুদের ছেলেরা সেকালে চণ্ডীতলায় মদ খাইয়া বীভৎস কাণ্ড করিয়া তুলিত। সাধারণ লোককে লইয়া তিনিই তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তারপর রামদাস গোস্বামীর সময়ে হইচই-এর ভিতরেও ছিল—বলো ভাই রাম নামের ধুয়া। তারপর সামাজিক ব্যাপার লইয়া অনেক হইচই হইয়া গেল। এই দেবুকে উপলক্ষ করিয়াই হইচই হইল তিনবার। সেটলমেন্ট লইয়া প্রথম। তারপর ধর্মঘট। তারপর এই বন্যার সাহায্য-সমিতি। প্রথমে তিনি দেবুর সম্বন্ধে আশা পোৰ্ষণ করিয়াছিলেন। ধর্মঘটের সময়েও সে প্রভাব তাহার উপরে ছিল। কিন্তু অকস্মাৎ এই পঞ্চায়েত উপলক্ষ করিয়া সেটা যেন উপিয়া গেল।
কালধৰ্ম, যুগধর্ম। শশীর শোচনীয় পরিণাম তাকে নিষ্ঠুর আঘাত দিয়া এ সম্বন্ধে চেতনা দিয়া গিয়াছে। তাই তিনি আর নিজেকে বিচলিত হইতে দেন না। প্রাণপণে নিজেকে সংযত করিয়া
কালের লীলাপ্রকাশ শুধু দ্রষ্টার মত দেখিয়া যাইতে বদ্ধপরিকর। যাহার যে পরিণতি হয় হউক, কাল যেরূপ আত্মপ্রকাশ করে করুক, তিনি দেখিবেন—শুধু নিশ্চেষ্টভাবে দেখিবেন।
নতুবা সেদিন বিশ্বনাথ যখন তাহার মুখের উপর বলিল—আপনার ঠাকুর এবং সম্পত্তির ব্যবস্থা আপনি করুন দাদু!—সেইদিন তিনি তাহাকে কঠোর শাস্তি দিতেন, কঠোর শাস্তি। পিতামহ হিসাবে তিনি দাবি করিতেন তাহার দেহের প্রতিটি অণুপরমাণুর মূল্য—যাহা তিনি দিয়াছিলেন তাঁহার পুত্র শশিশেখরকে, শশী দিয়া গিয়াছে তাহাকে।
ন্যায়রত্নের খড়মের শব্দ কঠোর হইয়া উঠিল। আপনার উত্তেজনা তিনি বুঝিতে পারিয়া গম্ভীরস্বরে ডাকিয়া উঠিলেন নারায়ণ! নারায়ণ!
বিশ্বনাথ কালকে পর্যন্ত স্বীকার করে না। সে বলে—কালের সঙ্গেই আমাদের লড়াই। এ কালকে শেষ করে আগামী কালকে নিয়ে আসারই সাধনা আমাদের।
মূৰ্খ! তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন—তা হলে কালের সঙ্গে যুদ্ধ বলছ কেন? কাল অনন্ত। তার এক খণ্ডাংশের সঙ্গে যুদ্ধ। আজকের কালকে চাও না, আগামী কালকে চাও! এ শাক্ত বৈষ্ণবের লড়াই। কালীরূপ দেখতে চাও না, কৃষ্ণরূপের পিপাসী! কিংবা ব্ৰজদুলালের পরিবর্তে দ্বারকানাথকে চাও!
বিশ্বনাথ বলিয়াছিল—কোনো নাথকেই আমি চাই না দাদু। তর্কের মধ্যে উপমার খাতিরে কাউকে চাই—একথা বললে আপনার লাভ কি হবে? নাথ আর সহ্য হচ্ছে না মানুষের, নাথের দল এই সুদীর্ঘকাল মানুষ যতবার উঠতে চেয়েছে—তাকে নাথত্বের চাপে নিষ্পেষিত করেছে। তাই আগামী কালের রূপ আমাদের অনাথের রূপ। নাথের উচ্ছেদেই হবে আজকের কালের অবসান।
কথাটা সত্য। পঞ্চগ্রামেও যতবার মানুষগুলি হইচই করিয়া উঠিয়াছে, ততবার জমিদার ধনী সমাজ-নেতারা তাহাদের দমন করিয়াছে। এ দেখিয়াও কি তোমার চেতনা হয় না বিশ্বনাথ যে, মানুষের জীবনোপ্যাস এমনভাবে আদিকাল হইতে ওই অনাথত্বের কালকে আনিতে চায় কিন্তু সে কাল আজও আসে নাই! কতকাল আজ অতীত হইয়া গেল—কত আগামী কাল আসিল, কিন্তু যে আগামী কালের কল্পনা তোমাদের সে কাল আসিল না। কেন আসিল না জান? কালের
সেই রূপে আসিবার কাল এখনও আসে নাই।
বিশ্বনাথ এইখানে যাহা বলে—তিনি তাহা কিছুতেই মানিতে পারেন না। তাহার সঙ্গে বিরোধ এইখানেই। গভীর বেদনায় নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণের মন আবার টনটন করিয়া উঠিল। আবার তিনি ডাকিলেন–নারায়ণ! নারায়ণ!
পোস্টাপিসের পিওন আসিয়া প্ৰণাম করিয়া দাঁড়াইল—চিঠি।
চিঠিখানি হাতে লইয়া ন্যায়রত্ন নাটমন্দির হইতে নামিয়া মুক্ত আলোকে ধরিলেন। বিশ্বনাথের চিঠি। ন্যায়রত্বের আজও চশমা লাগে না। তবে বৎসরখানেক হইতে আলোর একটু বেশি দরকার হয় এবং চোখ দুটি একটু সঙ্কুচিত করিয়া পড়িতে হয়। পোস্টকার্ডের চিঠি। ন্যায়রত্ন পড়িয়া একটু আশ্চর্য হইয়া গেলেনকল্যাণীয়াসু! কাহাকে লিখিয়াছে বিশু-ভাই? চিঠিখানা উল্টাইয়া ঠিকানা দেখিয়া দেখিলেন–জয়ার চিঠি। ন্যায়রত্ন অবাক হইয়া গেলেন। জয়াকে বিশ্বনাথ পোস্টকার্ডে চিঠি লিখিয়াছে! মাত্র কয়েক লাইন।
আমি ভাল আছি। আশা করি তোমরাও ভাল আছ। কয়েক দিনের মধ্যেই একবার ওখানে যাইব। ঠিক বাড়ি যাইব না। বন্যার সাহায্য-সমিতির কাজে যাইব, সঙ্গে আরও কয়েকজন যাইবেন। দাদুকে আমার অসংখ্য প্রণাম দিয়ে। তোমরা আশীৰ্বাদ জানিয়ো।
ইতি—বিশ্বনাথ।
ন্যায়রত্ন চিন্তিতভাবেই বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিলেন। পোস্টকার্ডের চিঠিখানা তাহাকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। সেদিন যখন বিশ্বনাথ তাঁহাকে বলিয়াছিল—জয়ার সঙ্গেও তাহার মতের মিল হইবে না, সেদিন তিনি এত বিচলিত হন নাই। মতের মিল তো নাই। জয়া তাহার হাতে-গড়া মহাগ্রামের মহামহোপাধ্যায় বংশের গৃহিণী। সমাজ ভাঙিয়াছে,ধর্ম বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে সারা পৃথিবীর লোভ, অনাচার, অত্যাচার—এ দেশের মানুষ জর্জরিত হইয়া ভয়াবহ পরধর্ম বা ধর্মহীন বৈদেশিক জীবন নীতি গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার অন্তঃপুরে আজও তাঁহার ধর্ম বাঁচিয়া আছে। জয়া অবিচলিত নিষ্ঠা এবং অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সঙ্গে তাহার দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। তাহার পৌত্র ভয়াবহ পরধর্ম গ্রহণ করিয়াছে—এই চিন্তায় যখন তিনি অধীর হন, তখন জয়ার দিকে চাহিয়া সান্ত্বনা পান। বিশ্বনাথ যখন তাহার সঙ্গে তর্ক করে কূটযুক্তিতে তাহাকে পরাজিত করিবার চেষ্টা করে, তখন তিনি গভীর তিতিক্ষায় নিজেকে সংযত করিয়া মহাকালের লীলার কথা ভাবিয়া নীরব হইয়া থাকেন—সেই নীরবতার মধ্যে মনে পড়ে জয়াকে। জয়ার জন্য দারুণ দুশ্চিন্তা হয়। আবার যখন বিশ্বনাথ নানা অজুহাতে পনের দিন, কুড়ি দিন অন্তর বাড়ি আসে, তখন ওই দুশ্চিন্তাই তাহার ভরসা হইয়া ওঠে। বিশ্বনাথ গোবিন্দজীর ঝুলন মানে না; কিন্তু সেই ঝুলনের অজুহাতে জয়ার সঙ্গে ঝুলন খেলা খেলিতে আসে। তাই জয়ার সঙ্গে মতে মিলিবে না বলিলেও ন্যায়রত্নের গোপন অন্তরে ভরসা ছিল। বহির সঙ্গে পতঙ্গের মিল আছে কি না কে জানে প্রাণশক্তির সঙ্গে দাহিকাশক্তির সম্বন্ধটাই বিরোধী সম্বন্ধ তবু পতঙ্গ আসে পুড়িয়া ছাই হইতে। জয়ার রূপের দিকে চাহিয়া তিনি আশ্বস্ত হন। কিন্তু আজ তিনি চিন্তিত হইলেন। বিশ্বনাথ জয়াকে পোস্টকার্ডে চিঠি লিখিয়াছে।
বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়া ন্যায়রত্ন ডাকিলেন-হলা রাজ্ঞী শান্তলে!
কেহ উত্তর দিল না। বাড়ির চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন—ভাড়ার ঘরে তালা ঝুলিতেছে, অন্য ঘরগুলির দরজাও বন্ধ, শিকল বন্ধ। ন্যায়রত্ন বিস্মিত হইলেন। জয়া তো এ সময়ে কোথাও যান না!
তিনি আবার ডাকিলেন—অজয়–অজু বাপি!
অজয় সাড়া দিল না—সাড়া দিল বাড়ির রাখালটা।–যাই আজ্ঞেন, ঠাকুর মশাই,… ওদিকের চালা হইতে ঘোড়াটা ঘুমন্ত অজয়কে কোলে করিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। খোকন ঘুমছে ঠাকুর মশাই!
–অজয়ের মা কোথায় গেল?
–আজ্ঞেন, বউঠাকুরণ যেয়েছেন আমাদের পাড়া।
—তোদের পাড়ায়?—ন্যায়রত্ন বিস্মিত হইয়া গেলেন। জয়া বাউরি-পাড়ায় গিয়াছে? তাহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।
ছোঁড়াটা বলিল–আজ্ঞেন, নোটন বাউরির ছেলেটা হাত-পা খিঁচছে—নোটনের বউ আইছিল—ঠাকুরের চরণামেত্তর লেগে। তাই গেলেন সেথা বউ-ঠাকুরণ!
–হাত-পা খিঁচছে? কি হয়েছে?
–তা জেনে না। বা-বাওড় লেগেছে হয়ত।
বা-বাওড় অর্থে ভৌতিক স্পর্শ। দুঃখের মধ্যেও ন্যায়রত্ন একটু হাসিলেন। এ বিশ্বাস ইহাদের কিছুতেই গেল না।
ঠিক এই সময়েই জয়া বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল। স্নান করিয়া ভিজা কাপড়ে ফিরিয়াছে। ন্যায়রত্ন চকিত হইয়া উঠিলেন—তুমি এই অবেলায় স্নান করলে? জয়া ক্লান্ত উদাস স্বরে উত্তর দিল ছেলেটি মারা গেল দাদু!
–মারা গেল?
–হ্যাঁ।
–কি হয়েছিল?
–জ্বর। কিন্তু এ রকম জ্বর তো দেখি নি দাদু।
ন্যায়রত্ন ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—আগে তুমি কাপড় ছাড় ভাই। তারপর শুনব।
জয়া তবু গেল না; বলিল কাল বিকেলবেলা থেকে সামান্য জ্বর হয়েছিল। সকালে উঠেও ছেলেটা খেলা করেছে। বললেজলখাবার-বেলা থেকে জ্বরটা চেপে এল। তারপরই ছেলে জ্বরে বেশ। ঘণ্টাখানেক আগে তড়কার মত হয়। তাতেই শেষ হয়ে গেল। শুনলাম দেখুড়েতেও নাকি পরশু একটি, কাল একটি ছেলে এমনিভাবেই মারা গিয়েছে। এদের পাড়াতে আরও তিন-চারটি ছেলের এমনি জ্বর হয়েছে। এ কি জ্বর দাদু?