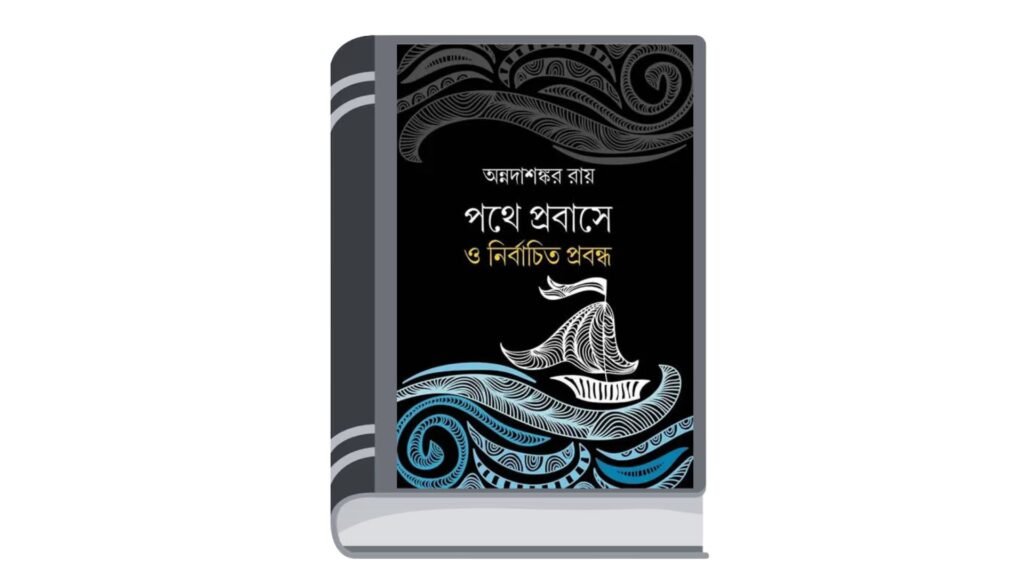পথে প্রবাসে
শ্রীসরলা দেবী
আয়ষ্মতীষু
ভূমিকা
আমি যখন বিচিত্রা পত্রিকায় প্রথম ‘পথে প্রবাসে’ পড়ি, তখন আমি সত্য সত্যই চমকে উঠেছিলুম। কলম ধরেই এমন পাকা লেখা লিখতে হাজারে একজনও পারেন না। শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্করের লেখা পড়লেই মনে হয় যে, তাঁর মনের কথা মন থেকে কলমের মুখে অবলীলাক্রমে চলে এসেছে। এ গদ্যের কোথাও জড়তা নেই এবং এর গতি সম্পূর্ণ বাধামুক্ত। আমরা যারা বাংলা ভাষায় মনোভাব প্রকাশ করতে চেষ্টা করি, আমরা জানি যে, ভাষাকে যুগপৎ স্বচ্ছ ও স্বচ্ছন্দ করা কতদূর আয়াসসাধ্য। সুতরাং, এই নবীন লেখকের সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত স্বপ্রকাশ ভাষার সঙ্গে যখন আমার প্রথম পরিচয় হয়, তখন যে আমি চমৎকৃত হয়েছিলুম, তাতে আর আশ্চর্য কী?
এই নবীন লেখকের ইন্দ্রিয় ও মন দুই-ই সমান সজাগ, আর তাঁর চোখে ও মনে যখন যা ধরা পড়ে তখনই তা ভাষাতেও ধরা পড়ে। আমি আগেই বলেছি যে, এই নবীন লেখকের ইন্দ্রিয় ও মন দুই-ই খোলা, আর প্রবাসে গিয়ে তাঁর চোখ-কান-মন আরও বেশ খুলে গিয়েছিল। তিনি বলেছেন, ‘আমার চোখজোড়া অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো ভূপ্রদক্ষিণে বেরিয়েছে।’ তিনি চোখ বুজে পৃথিবী ভ্রমণ করেননি, তার প্রমাণ ‘পথে প্রবাসে’-র পাতায় পাতায় আছে। আমরা, অর্থাৎ এ যুগের ভারতবাসীরা অর্ধসুপ্ত জাত; আমরা এই বিচিত্র পৃথিবীতে আসি, আর কিছুদিন থেকে চলে যাই। মাঝামাঝি সময়টা একরকম ধ্যানস্তিমিত লোচনেই কাটাই। এর কারণ নাকি আমাদের স্বাভাবিক বৈরাগ্য। আমাদের এই মনোভাবের প্রতি কটাক্ষ করে তিনি বলেছেন :
‘চুপ করে ঘরে বসে ভ্রমণকাহিনি লেখা ভালো, বৈরাগ্যবিলাসীর মতো সমস্ত ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ করে সর্ব প্রলোভনের অতীত হওয়া ভালো, সুরদাসের মতো দুটি চক্ষু বিদ্ধ করে ভুবনমোহিনী মায়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া ভালো।’—কিন্তু এ ভালো তিনি চাননি, কারণ তিনি বৈরাগ্যবিলাসী নন। এর ফলে তাঁর ‘পথে প্রবাসে’-র মধ্য থেকে, ‘মানবমানবীর শোভাযাত্রা থেকে কত রঙের পোশাক, কত ভঙ্গির সাজ, কত রাজ্যের ফুলের মতো মুখ’ পাঠকের চোখের সুমুখে আবির্ভূত হয়েছে।
শ্রীমান অন্নদাশঙ্কর লিখেছেন যে :
নতুন দেশে এলে কেবল যেসব ক-টা ইন্দ্রিয় সহসা চঞ্চল হয়ে ওঠে, তা নয়; সমস্ত মনটা নিজের অজ্ঞাতসারে খোলস ছাড়তে ছাড়তে কখন যে নতুন হয়ে ওঠে, তা দেশে ফিরে গেলে দেশের লোকের চোখে খট করে বাধে, নিজের চোখে ধরা পড়ে না।
সমগ্র ‘পথে প্রবাসে’ এই সত্যের পরিচয় দেয় যে ইউরোপের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ে লেখকের মন বিশেষ চঞ্চল ও ইন্দ্রিয় পুরোমাত্রায় সপ্রাণ হয়ে উঠেছে। এর কারণ, ইউরোপ আমাদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন দেশ। আর যিনি কখনো ও-দেশে গিয়েছেন, তাঁর কাছেই এ সত্য ধরা পড়েছে যে, সে-দেশটা ঘুমের দেশ নয়, মহাজাগ্রত দেশ। জাগরণ অবশ্য প্রাণের ধর্ম, আর তার বাহ্যলক্ষণ হচ্ছে দেহ ও মনের সক্রিয়তা। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা দেশের বিষয়ে বলেছেন যে, এ দেশটা স্বপ্ন দিয়ে তৈরি আর স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এককথায় যদি ইউরোপের বর্ণনা করতে হয় তো বলতে হয় যে, সে-দেশটা গতি দিয়ে তৈরি আর আশা দিয়ে ঘেরা।
প্রথম বয়সে যখন আমাদের ইন্দ্রিয় সব তাজা থাকে, আর যখন মন বাইরের রূপ বাইরের ভাব স্বচ্ছন্দে ও সানন্দে গ্রহণ করতে পারে, তখন ও-দেশের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে যেটা আমাদের দেশের যুবকরা সব প্রথম মনে ও প্রাণে অনুভব করে, সে হচ্ছে ও-জগতের প্রাণের লীলা। আমি যখন যৌবনে পদার্পণ করে তারপর ইউরোপে পদার্পণ করি তখন আমারও মন এই বিচিত্র প্রাণের লীলায় সাড়া দেয়। শ্রীমান অন্নদাশঙ্করের একটি কথায় আমাদের সকলেরই মন সায় দেয়, কারণ আমাদের লুপ্তপ্রায় পূর্বস্মৃতি সব আবার স্বরূপে দেখা দেয় :
‘ইউরোপের জীবনে যেন বন্যার উদ্দাম গতি সর্বাঙ্গে অনুভব করতে পাই, ভাবকর্মের শতমুখী প্রবাহ মানুষকে ঘাটে ভিড়তে দিচ্ছে না, এক-একটা শতাব্দীকে এক-একটা দিনের মতো ছোটো করে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সবচেয়ে স্বাভাবিক বোধ হচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদিনের প্রতি কাজে সংযুক্ত থেকে নারী ও নরের এক স্রোতে ভাসা।’ আজকালকার ভাষায় যাদের তরুণ বলে, তাদের মন এর প্রতি কথায় সাড়া দেবে। কারণ সে হচ্ছে যথার্থ তরুণ, যার হৃদয়মন সহজে ও স্বচ্ছন্দে যা স্বাভাবিক তাতে আনন্দ পায়। অর্থাৎ যারা কোনো শাস্ত্রের আবরণের ভিতর থেকে দুনিয়াকে দেখে না, সে শাস্ত্র দেশি-ই হোক আর বিলেতিই হোক; শঙ্করের বেদান্তই হোক আর Karl Marx-এর Das Kapital-ই হোক। শ্রীমান অন্নদাশঙ্কর আমার বিশ্বাস বিলেত নামক দেশটা চোখ চেয়ে দেখেছেন, পুস্তকের পত্র-আবডালের ভিতর থেকে উঁকি মেরে দেখেননি। এর ফলে তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত যথার্থ সাহিত্য হয়েছে।
‘পথে প্রবাসে’-র ভূমিকা আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে লিখতে বসেছি দু-কারণে। বাংলায় কোনো নতুন লেখকের সাক্ষাৎ পেলেই আমি স্বভাবত আনন্দিত হই। বলা বাহুল্য যে যিনি নতুন লিখতে আরম্ভ করেছেন তিনিই নতুন লেখক নন। যিনি প্রথমত লিখতে পারেন, আর দ্বিতীয়ত যাঁর লেখার ভিতর নূতনত্ব আছে, অর্থাৎ নিজের মনের বিশেষ প্রকাশ আছে, তিনি যথার্থ নতুন লেখক। ‘পথে প্রবাসে’-র লেখকের রচনায় এ দুটি গুণই ফুটে উঠেছে। আমরা যারা সাহিত্যজগতে এখন পেনশনপ্রার্থী—আমরা যে নতুন লেখকদেরও যথার্থ গুণগ্রাহী, একথাটা পাঠকসমাজকে জানাতে পারলে আমরা আত্মতুষ্টি লাভ করি।
দ্বিতীয়ত, আমি সত্য সত্যই চাই যে, বাংলার পাঠকসমাজে এ বইখানির প্রচার ও আদর হয়। এ ভ্রমণবৃত্তান্ত যে একখানি যথার্থ সাহিত্যগ্রন্থ এ বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই, এবং আমার বিশ্বাস সাহিত্যরসের রসিক মাত্রেই আমার সঙ্গে এ বিষয়ে একমত। তবে আমি আশা করি যে, ও-রসে বঞ্চিত কোনো প্রবীণ অথবা নবীন পাঠক পুস্তকখানিকে শাস্ত্রহিসেবে গণ্য করবেন না, কারণ তা করলেই সোনা ফেলে আঁচলে গেরো দেওয়া হবে। পৃথিবীতে জলবুদবুদের মতো নানা মত উঠছে ও মিলিয়ে যাচ্ছে। মনোজগতে এই-জাতীয় মতামতের উত্থান-পতনের ভিতরও অপূর্বতা আছে। কিন্তু এই সব মতামতকেই মহাবস্তু হিসেবে দেখলেই তা সাহিত্যপদভ্রষ্ট হয়ে শাস্ত্র হয়ে পড়ে। মতামতের বিশেষ কোনো মূল্য নেই, যদি না সে মতামতের পিছনে একটি বিশেষ মনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। আর এ লেখকের মতামতের পিছনে যে একটি সজীব মনের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
পূর্বকথা
আমার পথের আরম্ভ হল শ্রাবণের এক মধ্যরাত্রে—তিথি মনে নেই, কিন্তু শুক্লপক্ষের চাঁদ ছিল না।
ভারতবর্ষের দক্ষিণ ঘুরে ভারতবর্ষের বাইরে আমার পথ—কটক থেকে বম্বে, বম্বে থেকে লণ্ডন। বঙ্গোপসাগরের কূলে কূলে, পূর্বঘাট পর্বতমালার ধারে ধারে, চিল্কাহ্রদের কোল ঘেঁষে, গোদাবরীর বুক চিরে, হায়দরাবাদের তেপান্তরী মাঠ পেরিয়ে, পশ্চিমঘাট পর্বতমালার সানু জুড়ে আমার পথ—কটক, ওয়ালটেয়ার, বেজওয়াডা, সেকেন্দ্রবাদ, পুনা, বম্বে।
চিল্কার সঙ্গে এবার আমার দেখা আঁধার রাতের শেষ প্রহরে, সুন্দরী তখন আলোর স্বপ্ন দেখছে, তার দিগন্তজোড়া চোখের পাতায় যোগমায়ার অঞ্জন শ্বেতাভ হয়ে আসছে।
তমালবন দেখতে পেলুম না, কিন্তু চিল্কা থেকে গোদাবরী পর্যন্ত—হয়তো আরও দক্ষিণেও—তালীবনের অন্ত নেই। পথের একধারে পাহাড়ের পর পাহাড়, কিন্তু সব কটাই রুক্ষ, গায়ে তরুলতার শ্যাম প্রলেপ নেই, মাথায় নির্ঝরিণীর সরস স্নেহ নেই। পথের অন্যধারে খেত—কিন্তু বাংলার মতো তরল হরিৎ নয়।
প্রকৃতির এই বর্ণ-কার্পণ্য মানুষ তার পরিচ্ছদের বর্ণবৈচিত্র দিয়ে পুষিয়ে দিয়েছে। বিধাতা যেখানে শিল্পী সাজেন না মানুষকে সেখানে শিল্পী সাজতে হয়। মেয়েরা তো রঙিন ছাড়া পরেই না, পুরুষেরাও রঙিন পরে, এমন দেখতে পেলুম। এ দেশে অবরোধপ্রথা নেই, পথে ঘাটে সুবেশা সুকেশীর সাক্ষাৎ মেলে—‘সুকেশী’, কারণ এ দেশের মেয়েরা মাথায় কাপড় দেয় না, বিধবারা ছাড়া। এ দেশের জীবননাট্যে নারীর ভূমিকা নেপথ্যে নয়। দক্ষিণ ভারত নারীকে তার জন্মস্বত্ব থেকে বঞ্চিত না করে পুরুষকে সহজ হবার সুযোগ দিয়েছে। মুক্ত প্রকৃতির কোলে Wordsworth-এর Lucy যেমন ফুলের মতো ফুটেছিল, মুক্ত সমাজের কোলে মানুষও তেমনি মাধবীলতার মতো সুন্দর এবং সহকারের মতো সবল হতে হয়। বদ্ধ সমাজের অর্ধজীবী নারী-নর এহেন সত্য অস্বীকার করবে জানি, কিন্তু এ দেশের লোককে তর্কের দ্বারা বোঝাতে হবে না যে, মানুষ মানে পুরুষ ও মানুষ মানে নারী। নারীকে নিজের কাছে দুর্লভ করে আমরা উত্তর ভারতের লোক নিজেকে চিনতে ভুলেছি এবং যে আনন্দ আমরা হেলায় হারিয়েছি তার ধারণাও করতে কষ্ট পাচ্ছি। জন্মান্ধের যেমন আলোকবোধ থাকে না আমাদের তেমনি নারী-বোধ নেই, যা আছে তার নাম দিতে পারা যায় ‘কামিনী-জননী-বোধ’।
এখন যার নাম হায়দরাবাদের নিজামরাজ্য আগে তার নাম ছিল গোলকোণ্ডা। দেশটি সুদৃশ্য নয়, সুজলা সুফলাও নয়। যতদূর দৃষ্টি যায় কেবলি প্রান্তর, কদাচ কোথাও শৈলগুন্ঠিত, কদাচ কোথাও শস্যচিত্রিত। মাঝে মাঝে দেখা যায়—পাহাড়ের গায়ে দুর্গ। সন্দেহ হয় পাহাড়টাই দুর্গ, না দুর্গটাই পাহাড়। সমস্ত দেশটাই যেন একটা বিরাট ঘুমন্তপুরী—জনপ্রাণী নেই, গাছপালা নেই, পাখি-পাখাল নেই। তা বলে হায়দরাবাদের লোকসংখ্যা বড়ো অল্প নয়—প্রায় দেড় কোটি। এর পূর্বভাগে তেলেগুদের বাস, পশ্চিমভাগে মারাঠা ও কানাড়িদের। আর এ দেশের রাজার জাত মুসলমানেরা। রেলে যাদের দেখলুম তাদের বেশির ভাগ মুসলমান। উর্দুজবান জানা থাকলে ভ্রমণের অসুবিধা নেই।
কানাড়ি মেয়েদের অবরোধ নেই। তারা পুরুষের সঙ্গে পুরুষেরই মতো কঠিন খাটছে, এমন দেখা গেল। পথের ধারে ক্ষেত, কিসের ক্ষেত জানিনে, ধানের নয়, জোয়ারের কিংবা বাজরার কিংবা অন্য কিছুর। ছাব্বিশজন পুরুষের মাঝখানে হয়তো একজন মেয়েও খাটছে, ‘লজ্জাশরম’ নেই। নারী যে কর্মসহচরীও।
মহারাষ্ট্র পাহাড় পর্বতের দেশ—বহিঃপ্রকৃতি রুদ্র সুন্দর। নরনারীর মুখে-চোখে কমনীয়তা প্রত্যাশা করাই অন্যায়। বেশভূষায় নারী যেন পুরুষের দোসর। মালাবারে যেমন পুরুষেও কাছা দেয় না, মহারাষ্ট্রে তেমনি মেয়েমানুষেও কাছা দেয়। ফলে, পায়ের পশ্চাদ্ভাগ অনাবৃত ও কটু দেখায়। কিন্তু নারীকে যদি পুরুষের মতো স্বচ্ছন্দে চলাফেরা ও ছুটোছুটি করতে হয়, তবে এ ছাড়া উপায়ান্তর নেই। আমেরিকায় কর্মী-মেয়েরা পায়জামা পরে কাজ করে। মারাঠা মেয়েরা কর্মী-প্রকৃতি। তাদের অবরোধ নেই, তরুণীরা পায়ে হেঁটে স্কুল-কলেজে যাচ্ছে, বয়স্কারা attaché case হাতে বাজার করতে বেরিয়েছেন, কত মেয়ে একাকী ট্রামে উঠছে, ট্রেনে বেড়াচ্ছে, ভয়ডর নেই, লজ্জা সংকোচ নেই, পুরুষের সঙ্গে সহজ ব্যবহার। পায়ে বর্মা চটির মতো হালকা খোলা চটি, পরনে নীল বা বেগুনি—একটু গাঢ় রঙের—ঈষৎ কোঁচা কাছা দেওয়া শাড়ি, পিঠের ওপর একরঙা শাড়ির বহুরঙা আঁচল চওড়া করে বিছানো, মাথায় কাপড় নেই, কবরীতে ফুলের পাপড়ি গোঁজা কিংবা ফুলের মালা গোল করে জড়ানো, হৃষ্টপুষ্ট সুবলয়িত দেহবয়বে অল্প কয়েক খানা অলংকার, প্রশস্ত সুগোল মুখমন্ডলে সুপ্রতিভ পুরুষকারের ব্যঞ্জনা—মহারাষ্ট্রের মেয়েদের দেখে মোটের ওপর মহাসম্ভ্রম জাগে। তন্বী ওদের মধ্যে চোখে পড়ল না। কিন্তু পৃথুলাও চোখে পড়ে না। সুস্থ সবল ও সপ্রতিভ বলে এদের অধিকাংশকেই সুশ্রী দেখায়, কিন্তু ‘রমণীয়’ দেখায় বললে বোধ হয় বেশি বলা হয়। এদের চালচলনে-চেহারায় পৌরুষের ছায়া পড়েছে বলে এদের নারীত্বের আকর্ষণ কমেছে এমনও বলা যায় না। পুরুষের কাছে নারী যদি কাবুলি পায়জামার ওপরে গেরুয়া আলখাল্লা ও গাড়োয়ানি ফ্যাশানের দশ আনা ছ-আনা চুলের ওপরে চিমনি প্যাটার্নের সিল্ক টুপি পরে, তবু পুরুষের কাছে সে এমনি চিত্তাকর্ষক থাকবে। মারাঠা পুরুষের চোখে মারাঠা মেয়েদের যে অপূর্ব রমণীয় ঠেকে এ তো স্বতঃসিদ্ধ, আমার চোখেও তাদের নারীর মতোই ঠেকেছে। দৃষ্টিকটু বোধ হচ্ছিল কেবল শ্রমিক-শ্রেণির মেয়েগুলিকে; মালকোচ্চা মারা পালোয়ানদের বুকে একটুকরো জামার উপর ময়লা নীল কাপড় জড়িয়ে বাঁধলে যেমন দেখাত এদেরও অনেকটা তেমনি দেখায়। যেমন এদের ভারবহন ক্ষমতা, তেমনি এদের ছুটে চলার ক্ষিপ্রতা। আমাদের অঞ্চলের পুরুষরা পর্যন্ত এদের তুলনায় কুঁড়ে।
মারাঠা পুরুষদের বাহুবল সম্বন্ধে যে প্রসিদ্ধি আছে সেটা সত্য নয়, অন্তত আপাতদৃষ্টিতে। এদের মনের বল কিন্তু অসাধারণ। মুখের ওপর আত্মসম্মানবত্তার এমন সুস্পষ্ট ছাপ অন্য কোনো জাতের মধ্যে লক্ষ্য করিনি। অর্থনৈতিক জীবনযুদ্ধে কিন্তু মারাঠারা গুজরাটিদের কাছে হটতে লেগেছে। বম্বে শহরটার স্থিতি মহারাষ্ট্রেরই জিওগ্রাফিতে বটে, বম্বে শহরের জিওগ্রাফিতে কিন্তু মহারাষ্ট্রের স্থিতি গলির বস্তিতে আর গুজরাটের স্থিতি সড়কের চারতলায়। বাঙালি বাঘের ঘরে যেমন মাড়োয়ারি ঘোঘের বাসা, মারাঠা বাঘের ঘরে তেমনি গুজরাটি ঘোঘের বাসা। গুজরাটি মানে পারসিও বুঝতে হবে। পারসিদেরও মাতৃভাষা গুজরাটি। ইদানীং অবশ্য ওরা কায়বাক্যে ইংরেজ হবার সাধনায় লেগেছে।
গুজরাটি জাতটার প্রতি আমার কেমন একরকম পক্ষপাত আছে। শুনেছি ওদের সাহিত্য বাংলা সাহিত্যেরই ঠিক নীচে এবং রবিহীন বাংলা সাহিত্যের সমকক্ষ। গান্ধীর মতো ভাবশিল্পী যে জাতির মনের স্তন্যে পুষ্ট সে জাতির মনকে বাঙালিমনের অনুজ ভাবা স্বাভাবিক। গুজরাটিরা পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে নানা দেশের ধনের সঙ্গে সঙ্গে নানা দেশের মনেরও আমদানি করছে এবং বিদেশি মনের সোনার কাঠি আমাদের মতো ওদের সাহিত্যকেও সোনা করে দিচ্ছে। তফাত এই যে, আমরা যা বইয়ের মারফত পাই ওরা তা সংসর্গের দ্বারা পায়।
গুজরাটি পুরুষরা যে পরম কষ্টসহিষ্ণু ও কর্মঠ এ তো আমরা দেশে থেকেও জানি, তাদের ব্যবসায়বুদ্ধিও বহুবিদিত। গুজরাটি মেয়েদের মধ্যেও এইসব গুণ আছে কি না জানিনে। তাদের পর্দা নেই, তবে উত্তর ভারতের সঙ্গে সংস্পৃষ্ট বলে গতিবিধির স্বাধীনতা মারাঠাদের চেয়ে কিছু কম। গুজরাটি মেয়েদের পরিচ্ছদ-পারিপাট্য আমাদেরই মেয়েদের মতো; কাপড় পরার ভঙ্গিতে ইতরবিশেষ থাকলেও মোটের ওপর মিল আছে। মারাঠা মেয়েরা সচরাচর যে অন্তর্বাস পরে তার ঝুল বুকের নীচে পর্যন্ত—কোমরের কাছটা অনাবৃত ও শাড়ি দিয়ে ঢাকতে হয়। গুজরাটি মেয়েরা কিন্তু আপাদচুম্বী অন্তর্বাস পরে তার ওপরে শাড়ি পরে। শুনেছি আমাদের মেয়েদের অন্তর্বাস পরা শুরু হয় গুজরাটেরই অনুকরণে ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পত্নীর দ্বারা।
আমাকে সকলের চেয়ে মুগ্ধ করল গুজরাটি মেয়েদের দেহের তনুত্ব ও মুখের সৌকুমার্য। মারাঠাদের সঙ্গে এদের অমিল যেমন স্পষ্ট, বাঙালিদের সঙ্গে এদের মিলও তেমনি স্পষ্ট। তবে বাঙালি মেয়েদের দেহের গড়নের চেয়ে গুজরাটি মেয়েদের দেহের গড়ন অনেক বেশি সুসমঞ্জস; এবং বাঙালি মেয়েদের মুখশ্রীতে যেমন স্নিগ্ধতার মাত্রাধিক্য, গুজরাটি মেয়েদের মুখশ্রীতে তেমন নয়।
পারসিরাই হচ্ছে এ অঞ্চলের Leaders of fashion। তারা কাঞ্চনকুলীন তো বটেই, রীতিরুচিতেও অভিজাত। পারসি মেয়েদের জাঁকালো বেশভূষার সঙ্গে ইঙ্গবঙ্গদের পর্যন্ত তুলনা করা চলে না। অন্তত তিনপ্রস্থ অন্তর্বাস বাইরে থেকে লক্ষ করতে পারা যায়; প্রৌঢ়াদেরও শাড়ির বাহার আছে। মারাঠাদের যেমন আঁচলের বাহার পারসিদের তেমনই পাড়ের বাহার। হালকা রঙের আদর এ অঞ্চলে নেই। হাজার হাজার নানা বয়সি মেয়ের মধ্যে মাত্র কয়েক জন কিশোরীকেই হালকা রঙের শাড়ি পরতে দেখলুম। সাদার চল একমাত্র গুজরাটিদের মধ্যেই পরিলক্ষ্য। বলতে ভুলে গেছি, গুজরাটি ও পারসিরা মাথায় কাপড় দেয়, কিন্তু ঘোমটার মতো করে নয়, খোঁপার সঙ্গে এঁটে। গহনার বাহুল্য নেই—আমাদের মেয়েদের তুলনায় এরা নিরলংকার। পারসি মেয়েরা ইংরেজি জুতো পায়ে দেয়—গুজরাটি মেয়েরা সচরাচর কোনো জুতোই পায়ে দেয় না—মারাঠা মেয়েরা চটি পরে।
বম্বে শহর কলকাতার চেয়ে আকারে ছোটো কিন্তু প্রকারে সুন্দর। প্রায় চারিদিকে সমুদ্র, অদূরে পাহাড়, ভিতরেও ‘মালাবার হিল’ নামক অনুচ্চ পাহাড়, তার ওপরে বড়ো বড়ো লোকের সাজানো হর্ম্য। শহরের রাস্তাগুলি যেন প্লান করে তৈরি। বম্বেবাসীদের রুচির প্রশংসা করতে হয়—টাকা তো কলকাতার মাড়োয়ারিদেরও আছে, কিন্তু তাদের রুচির নিদর্শন তো বড়োবাজারের ‘ইটের পর ইট’! বম্বের প্রত্যেকখানি বাড়িরই যেন বিশেষত্ব আছে—প্রত্যেকেরই ডিজাইন স্বতন্ত্র। শহরটা ছবিল কিন্তু আমার মনে হয় এ সত্ত্বেও বম্বে ভারতীয় নগর-স্থাপত্যের ভালো নিদর্শন নয়। বম্বের বাস্তুশিল্পের গায়ে যেন ইংরেজি গন্ধ পেলুম, তাও খাঁটি ইংরেজি নয়। তবু কলকাতার নাই-শিল্পের চেয়ে বম্বের কানা শিল্প ভালো।
১
ভারতবর্ষের মাটির ওপর থেকে শেষবারের মতো পা তুলে নিলুম আর সদ্যোজাত শিশুর মতো মায়ের সঙ্গে আমার যোগসূত্র এক মুহূর্তে ছিন্ন হয়ে গেল। একটি পদক্ষেপে যখন সমগ্র ভারতবর্ষের কক্ষচ্যুত হয়ে অনন্ত শূন্যে পা বাড়ালুম তখন যেখান থেকে পা তুলে নিলুম সেই পদ-পরিমাণ ভূমি যেন আমাকে গোটা ভারতবর্ষেরই স্পর্শ-বিরহ অনুভব করিয়ে দিচ্ছিল; প্রিয়জনের আঙুলের ডগাটুকুর স্পর্শ যেমন প্রিয়জনের সকল দেহের সম্পূর্ণ স্পর্শ অনুভব করিয়ে দেয়, এও যেন তেমনি।
জাহাজে উঠে বম্বে দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি করুণ। এত বড়ো ভারতবর্ষ এসে এতটুকু নগরপ্রান্তে ঠেকেছে, আর কয়েক মুহূর্তে ওটুকুও স্বপ্ন হবে, তখন মনে হবে আরব্য উপন্যাসের প্রদীপটা যেমন বিরাটাকার দৈত্য হয়ে আলাদিনের দৃষ্টি জুড়েছিল, ভারতবর্ষের মানচিত্রখানা তেমনি মাটি জল ফুল পাখি মানুষ হয়ে আজন্ম আমার চেতনা ছেয়েছিল, এত দিনে আবার যেন মানচিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে।
আর মানচিত্রে যাকে ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার মাঝখানে গোস্পদের মতো দেখাত সে-ই এখন হয়েছে পায়ের তলার আরব সাগর, পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ কোনো দিকে চক্ষু তার অবধি পায় না। ঢেউগুলো তার অনুচর হয়ে আমাদের জাহাজখানাকে যেন গলাধাক্কা দিতে দিতে তার চৌকাঠ পার করে দিতে চলেছে। ঋতুটার নাম বর্ষা ঋতু, মনসুনের প্রভঞ্জনাহুতি পেয়ে সমুদ্র তার শতসহস্র জিহ্বা লকলক করছে, জাহাজখানাকে একবার এদিকে কাত করে একবার ওদিকে কাত করে যেন ফুটন্ত তেলে পাঁপরের মতো উলটে-পালটে ভাজছে।
জাহাজ টলতে টলতে চলল, আর জাহাজের অধিকাংশ যাত্রী-যাত্রিণী ডেক ছেড়ে শয্যা আশ্রয় করলেন। অসহ্য সমুদ্রপীড়ায় প্রথম তিন দিন আচ্ছন্নের মতো কাটল, কারোর সঙ্গে দেখা হবার জো ছিল না, প্রত্যেকেই নিজের নিজের ক্যাবিনে শয্যাশায়ী। মাঝে মাঝে দু-একজন সৌভাগ্যবান দেখা দিয়ে আশ্বাসন করেন, ডেকের খবর দিয়ে যান। আর ক্যাবিন স্টুয়ার্ড খাবার দিয়ে যায়। বলা বাহুল্য জিহ্বা তা গ্রহণ করতে আপত্তি না-করলেও উদর তা রক্ষণ করতে অস্বীকার করে।
ক্যাবিনে পড়ে পড়ে বমনে ও উপবাসে দিনের পর রাত রাতের পর দিন এমন দুঃখে কাটে যে, কেউ-বা ভাবে মরণ হলেই বাঁচি, কেউ-বা ভাবে মরতে আর দেরি নেই। জানিনে হরবল্লভের মতো কেউ ভাবে কি না যে, মরে তো গেছি, দুর্গানাম করে কী হবে। সমুদ্রপীড়া যে কী দুঃসহ তা ভুক্তভোগী ছাড়া অপর কেউ ধারণা করতে পারবে না। হাতের কাছে রবীন্দ্রনাথের চয়নিকা, মাথার যন্ত্রণায় অমন লোভনীয় বইও পড়তে ইচ্ছা করে না। ইচ্ছা করে কেবল চুপ করে পড়ে থাকতে, পড়ে পড়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে।
সদ্য-দুঃখার্ত কেউ সংকল্প করে ফেললেন যে, এডেনে নেমেই দেশে ফিরে যাবেন, সমুদ্রযাত্রার দুর্ভোগ আর সইতে পারবেন না। তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল এডেন থেকে দেশে ফিরে যেতে চাইলেও উটের পিঠে চড়ে মরুভূমি পেরিয়ে পারস্যের ভিতর দিয়ে ফেরবার যখন উপায় নেই তখন ফিরতে হবে সেই সমুদ্রপথেই। আমরা অনেকেই কিন্তু ঠিক করে ফেললুম মার্সেলসে নেমে প্যারিসের পথে লণ্ডন যাব।
আরব সাগরের পরে যখন লোহিত সাগরে পড়লুম তখন সমুদ্রপীড়া বাসি হয়ে গেছে। আফ্রিকা-আরবের মধ্যবর্তী এই হ্রদতুল্য সমুদ্রটি দুর্দান্ত নয়, জাহাজে থেকে থেকে জাহাজটার ওপর মায়াও পড়ে গেছে; তখন না মনে পড়ছে দেশকে, না ধারণা করতে পারা যাচ্ছে বিদেশকে। কোথা থেকে এসেছি ভুলে গেছি, কোথায় যাচ্ছি বুঝতে পারছিনে; তখন গতির আনন্দে কেবল ভেসে চলতেই ইচ্ছা করে, কোথাও থামবার বা নামবার সংকল্প দূর হয়ে যায়।
বিগত ও আগতের ভাবনা না-ভেবে উপস্থিতের ওপরে দৃষ্টি ফেললুম—আপাতত আমাদের এই ভাসমান পান্থশালাটায় মন ন্যস্ত করলুম। খাওয়া-শোয়া লেখা-পড়া-গল্প করার যেমন বন্দোবস্ত যে কোনো বড়ো হোটেলে থাকে এখানেও তেমনি, কেবল ক্যাবিনগুলো যা যথেষ্ট বড়ো নয়। ক্যাবিনে শুয়ে থেকে সিন্ধু-জননীর দোল খেয়ে মনে হয় খোকাদের মতো দোলনায় শুয়ে দুলছি। সমুদ্রপীড়া যেই সারল ক্যাবিনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অমনি কমল। শোবার সময়টা ছাড়া বাকি সময়টা আমরা ডেকে কিংবা বসবার ঘরে কাটাতুম। ডেকে চেয়ার ফেলে বসে কিংবা পায়চারি করতে করতে সমুদ্র দেখে দেখে চোখ শ্রান্ত হয়ে যায়; চারদিকে জল আর জল, তাও নিস্তরঙ্গ, কেবল জাহাজের আশেপাশে ছাড়া ঢেউয়ের অস্তিত্ব নেই, যা আছে তা বাতাসের সোহাগ চুম্বনে জলের হৃদয়স্পন্দন। বসবার ঘরে অর্ধশায়িত থেকে খোশগল্প করতে এর চেয়ে অনেক ভালো লাগে।
লোহিত সাগরের পরে ভূমধ্যসাগর। দুয়ের মাঝখানে যেন একটি সেতু ছিল, নাম সুয়েজ যোজক। এই যোজকের ঘটকালিতে এশিয়া এসে আফ্রিকার হাত ধরেছিল। সম্প্রতি হাতের জোড় খুলে দুই মহাদেশের মাঝখানে বিয়োগ ঘটিয়ে দেওয়া হয়েছে। যার দ্বারা তা ঘটল তার নাম সুয়েজ ক্যানেল। সুয়েজ ক্যানেল একদিকে বিচ্ছেদ ঘটাল বটে, কিন্তু অন্যদিকে মিলন ঘটাল—লোহিতের সঙ্গে ভূমধ্যের মিলন যেন ভারতের সঙ্গে ইউরোপের মিলন। কলম্বাস যা পারেননি, লেসেপস তা পারলেন। ভূমধ্য ও লোহিতের মধ্যে কয়েক শত মাইলের ব্যবধান, ওইটুকুর জন্য ভূমধ্যের জাহাজকে লোহিতে আসতে বহু সহস্র মাইল ঘুরে আসতে হত। মিশরের রাজারা কোন যুগ থেকে এর প্রতিকারের উপায় খুঁজছিলেন। উপায়টা দেখতে গেলে সুবোধ্য। ভূমধ্য ও লোহিতের মধ্যবর্তী ভূখন্ডটাতে গোটা কয়েক হ্রদ চিরকালই আছে, এই হ্রদগুলোকে দুই সমুদ্রের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিলেই সেই জলপথ দিয়ে এক সমুদ্রের জাহাজ অন্য সমুদ্রে যেতে পায়। কল্পনাটা অনেক কাল আগের, কিন্তু সেটা কার্যে পরিণত হতে হতে গত শতাব্দীর দুই-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়ে গেল। ক্যানেলটিতে কলাকুশলতা কী পরিমাণ আছে তা স্থপতিরাই জানেন, কিন্তু অব্যবসায়ী আমরা জানি যাঁর প্রতিভার স্পর্শমণি লেগে একটা বিরাট কল্পনা একটা বিরাট কীর্তিতে রূপান্তরিত হল সেই ফরাসি স্থপতি লেসেপস একজন বিশ্বকর্মা; তাঁর সৃষ্টি দূরকে নিকটে এনে মানুষের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর করেছে। যান্ত্রিক সভ্যতার শত অপরাধ যাঁরা নিত্য স্মরণ করেন, এই ভেবে তাঁরা একটি অপরাধ মার্জনা করুন।
সুয়েজ ক্যানেল আমাদের দেশের যেকোনো ছোটো নদীর মতোই অপ্রশস্ত, এতে বড়োজোর দুখানা জাহাজ পাশাপাশি আসা-যাওয়া করতে পারে, কিন্তু ক্যানেল যেখানে হ্রদে পড়েছে সেখানে এমন সংকীর্ণতা নেই। ক্যানেলটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি দিকে নানান রকমের গাছ, যত্ন করে লাগানো, যত্ন করে রক্ষিত; অন্যদিকে ধু-ধু করা মাঠ, শ্যামলতার আভাসটুকুও নেই। ক্যানেলের দুই দিকেই পাথরের পাহাড়, যেদিকে মিশর সেই দিকেই বেশি। এই পাহাড়গুলিতে যেন জাদু আছে, দেখলে মনে হয় যেন কোনো কিউবিস্ট এদের আপন খেয়ালমতো জ্যামিতিক আকার দিয়েছে আরএক-একটা পাথর কুঁদে গড়েছে।
ক্যানেলটি যেখানে ভূমধ্যসাগরে পড়েছে সেখানে একটি শহর দাঁড়িয়ে গেছে, নাম পোর্ট সৈয়দ। জাহাজ থেকে নেমে শহরটায় বেড়িয়ে আসা গেল। শহরটার বাড়িঘর ও রাস্তাঘাট ফরাসি প্রভাবের সাক্ষ্য দেয়। কাফেতে খাবার সময় ফুটপাথের ওপর বসে খেতে হয়, রাস্তায় চলবার সময় ডান দিক ধরে চলতে হয়। পোর্ট সৈয়দ হল নানা জাতের নানা দেশের মোসাফিরদের তীর্থস্থল; কাজেই সেখানে তীর্থের কাকের সংখ্যা নেই, ফাঁক পেলে একজনের ট্যাঁকের টাকা আর একজনের ট্যাঁকে ওঠে।
পোর্ট সৈয়দ মিশরের অঙ্গ। মিশর প্রায় স্বাধীন দেশ। ইউরোপের এত কাছে বলে ও নানা জাতের পথিক-কেন্দ্র বলে মিশরিরা ইউরোপীয়দের সঙ্গে বেশি মিশতে পেরেছে, তাদের বেশি অনুকরণ করতে শিখেছে, তাদের দেশে অনায়াসে যাওয়া-আসা করতে পারছে। ফলে ইউরোপীয়দের প্রতি তাদের অপরিচয়ের ভীতি বা অতিপরিচয়ের অবজ্ঞা নেই, ইউরোপীয়দের স্বাধীন মনোবৃত্তি তাদের সমাজে ও রাষ্ট্রে সঞ্চারিত হয়েছে।
পোর্ট সৈয়দ ছেড়ে আমরা ভূমধ্যসাগরে পড়লুম। শান্তশিষ্ট বলে ভূমধ্যসাগরের সুনাম আছে। প্রথম দিন কতক চতুর ব্যবসাদারের মতো ভূমধ্যসাগর ‘Honesty is the best policy’ করলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভদ্রতা রক্ষা করলে না। আর একবার করে কেউ কেউ শয্যাশায়ী হলেন। অধিকাংশকে মার্সেলসে নামতেই হল। পোর্ট সৈয়দ থেকে মার্সেলস পর্যন্ত জল ছাড়াও দুটি দৃশ্য ছাড়া দেখবার আর কিছু নেই। প্রথমটি ইটালি ও সিসিলির মাঝখানে মেসিনা প্রণালী দিয়ে যাবার সময় দুই ধারের পাহাড়ের সারি। দ্বিতীয়, স্ট্রম্বলি আগ্নেয় গিরির কাছ দিয়ে যাবার সময় পাহাড়ের বুকে রাবণের চিতা।
মার্সেলস ভূমধ্যসাগরের সেরা বন্দর ও ফরাসিদের দ্বিতীয় বড়ো শহর। ইতিহাসে এর নাম আছে, বন্দে মাতরম ‘La Marseillaise’ এই নগরেই জন্ম। কাব্যে এ অঞ্চলের নাম আছে, ফরাসি সহজিয়া কবিদের (troubadour) প্রিয়ভূমি এই সেই Provence —বসন্ত যেখানে দীর্ঘস্থায়ী ও জ্যোৎস্না যেখানে স্বচ্ছ। এর পূর্ব দিকে সমুদ্রের কূলে কূলে ছোটো ছোটো অসংখ্য গ্রাম, সেই সব গ্রামে গ্রীষ্মযাপন করতে পৃথিবীর সব দেশের লোক আসে। Bandol নামক তেমনি একটি গ্রামে আমরা একটি দুপুর কাটালুম। মোটরে করে পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে সেখানে যেতে হয়। পাহাড়ের ওপর থেকে মার্সেলসকে দেখলে মনে হয় যেন সমুদ্র তাকে সাপের মতো সাতপাকে জড়িয়ে বেঁধেছে। মার্সেলস শহরটাও পাহাড় কেটে তৈরি, ওর একটা রাস্তার সঙ্গে আরেকটা রাস্তা সমতল নয়, কোনো রাস্তায় ট্রামে করে যেতে ডান দিকে মোড় ফিরলে একেবারে রসাতল, কোনো রাস্তায় চলতে চলতে বাঁ-দিকে বেঁকে গেলে সামনে যেন স্বর্গের সিঁড়ি। মার্সেলসের অনেক রাস্তার দু-ধারে গাছের সারি ও তার ওপারে ফুটপাথ।
মার্সেলস থেকে প্যারিসের রেলপথে রাত কাটল। প্যারিস থেকে রেলপথে ক্যালে, ক্যালে থেকে জলপথে ডোভার এবং ডোভার থেকে রেলপথে লণ্ডন।
২
লণ্ডনের সঙ্গে আমার শুভদৃষ্টি হল গোধূলি লগ্নে। হতে-না-হতেই সে চক্ষু নত করে আঁধারের ঘোমটা টেনে দিলে। প্রথম পরিচয়ের কুমার-বিস্ময় গোড়াতেই ব্যাহত হয়ে যখন অধীর হয়ে উঠল তখন মনকে বোঝালুম, এখন এ তো আমারই। আবরণ এর দিনে দিনে খুলব।
পরের দিন সকালে উঠে দেখি আকাশ কলের ধোঁয়ায় মুখ কালো করে ছিঁচকাঁদুনে ছেলের মতো যখন-তখন চোখের জল ঝরাচ্ছে। সূর্যদেবের ঠিকঠিকানা নেই। সম্ভবত তিনি কাঁদুনেটাকে খেপিয়ে দিয়ে মাস্টারের ভয়ে দুষ্টুছেলের মতো ফেরার হয়েছেন। লণ্ডনের চিমনিওয়ালা বাড়িগুলো চুরুটখোরদের মতো মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আকাশের দিকে চেয়ে হাসছে, আর যে দু-চারটে গাছপালার বহু কষ্টে সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তারা আমাদের অসূর্যম্পশ্যাদের মতো চিকের আড়ালে দাঁড়িয়ে পাতা খস খস করতে করতে হতভাগ্য আকাশটার দিকে ছলছল চোখে তাকাচ্ছে।
ক্রমে জানলুম এইটেই এখানকার সরকারি আবহাওয়া। মাঝে মাঝে এর নিপাতন হয়, গ্রীষ্মকালে এর ব্যতিক্রম হয়, কিন্তু সারা শীতকালটা নাকি এমনি চলে। কদাচ কোনোদিন আকাশের উঠোন নিকিয়ে নির্মল করা হলে রুপালি সূর্য উঠে ধূমলা নগরীকে বলে, ‘গুডমর্নিং’। অমনি ঘরে ঘরে খবর রটে, পথে পথে পথিক দেখা দেয়, চেনামুখ চেনামুখকে বলে, ‘হাও লাভলি! আজ সারাদিন যদি এমনি থাকে…!’ মুখের কথা মুখ থেকে না-মিলাতেই সূর্য বলে এখন আসি; বৃষ্টি বলে এবার নামি; একদল পথিক ভাবে ছাতা না-এনে কী বোকামি করেছি, আরেক দল পথিক ভাবে ভাগ্যে রেনকোটখানা সঙ্গে ছিল। ইংল্যাণ্ডের ওয়েদার এমনই খোশমেজাজি যে, খবরের কাগজওয়ালারা প্রতিদিন তার ভাবী চালের খবর নেয় ও কাগজের সর্বপ্রথম পৃষ্ঠায় সর্বোচ্চে ছেপে দেয়—কাল বাতাস প্রথমে পশ্চিম থেকে ও পরে নৈর্ঋত থেকে বইবে, ক্রমশ তার বেগ বাড়বে, সূর্য গা-ঢাকা দেবে, কিন্তু বৃষ্টি জোরে পড়বে না।
এ গেল লণ্ডনের অন্তরিক্ষের খবর। জলস্থলের বৃত্তান্ত বলা যাক।
লণ্ডন শহর টেমস নদীর কূলে। কিন্তু গঙ্গা গোদাবরীর দেশের লোক আমি টেমসকে নদী বলি কেমন করে? লণ্ডনের যেকোনো দুটো চওড়া রাস্তাকে পাশাপাশি করলে টেমসের চেয়ে এক এক জায়গায় কম অপ্রশস্ত হয় না। ছোটো হলে কী হয়, নদীটি নৌবাহ্য। বড়ো বড়ো জাহাজকে অনায়াসে কোল দেয়, বলিষ্ঠ শিশুর তন্বঙ্গী মায়ের মতো। লণ্ডনের যোজনজোড়া জটায় জাহ্নবীর মতো এঁকেবেঁকে নির্গমের পথ খুঁজছে, পিছু হটছে, মোড় ফিরছে। শহরের বাইরে তার উভয় তটে ছবির মতো বন, তার কূল সবুজ মখমলে মোড়া। কিন্তু শহরের ভিতর তার জল কলকাতার গঙ্গার মতো বিবর্ণ, কাশীর গঙ্গার মতো স্বচ্ছ নয়। তার ধারে দাঁড়ালে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে; বাতাস তো নেই, আছে ধোঁয়া। ঝাপসা চোখে দু-ধারের দৃশ্য দেখি, শিপিয়া-কালো ইট-কাঠের স্তূপ, তাদের গায়ে বড়ো বড়ো হরফে বিজলি আলোর বিজ্ঞাপন—‘মদ’ কিংবা ‘সিগরেট’ কিংবা ‘খবরের কাগজ’। ওই তিনটে তিন রকমের বিষ এদেশে প্রচুর বিক্রি হয়।
লণ্ডন শহর গোটা সাত-আট কলকাতার সমান। আয়তন ছাড়া নতুন কিছু দেখবার নেই। সেই ট্রাম সেই বাস সেই ট্যাক্সি সেই ট্রেন সেই গলি সেই বস্তি সেই মাঠ সেই প্রাসাদ। প্রভেদ এই যে, সমস্তই সুপারলেটিভ, সমস্তই অতিকায়। লণ্ডনের দীনতমঅঞ্চলগুলিও প্রত্যেকটি যেন এক-একটি দক্ষিণ কলকাতা, ঐশ্বর্যে অতটা না-হোক পরিচ্ছন্নতায় অতটা। এত বড়ো শহর কিন্তু সেই অনুপাতে কোলাহলমুখর নয়। অবশ্য কলের কর্কশ আওয়াজে বাড়ির ভিত পর্যন্ত নড়ে এবং মোটরের দাপাদাপিতে রাস্তাগুলোর বুক দুড়দুড় করে, কিন্তু জনতার মুখে কথা নেই। ভিড়ের মধ্যে ফিসফিস করলেও শোনা যায়। ফেরিওয়ালার রকমারি হাঁক নেই, তার চলন্ত বিজ্ঞাপন পড়ে বুঝতে হয় সে কী বেচতে চায় ও কত দামে। দুধওয়ালা ঘরে ঘরে দুধ বিলি করে যাবার সময় এমন সুরে ‘milk’ বলে যে, শুনলে মনে হয় কোকিলের ‘কু—উ’। ডাকপিয়োন কাঠঠোকরার মতো দরজায় দুই ঠোক্কর দিলে বুঝতে হয় দরকারি চিঠি এসেছে, রুটিওয়ালা, মাংসওয়ালা, কয়লাওয়ালা ইত্যাদি প্রত্যেকেরই নিজস্ব ‘চিচিং ফাঁক’ আছে, সেই সংকেত শুনলে বন্ধ দুয়ার আপনি খুলে যায়, অর্থাৎ বাড়ির ঝি দরজা খুলে দেয়। এককথায় বলতে গেলে এখানে হাটের মধ্যে তেমন হট্টগোল নেই যেমন আমাদের দেশের ঘরে ঘরে। কিন্তু এতটা নিস্তব্ধতা কি স্বাভাবিক না সুন্দর? সুর করে ‘দই নেবে গো, মিষ্টি দই’ হাঁকতে হাঁকতে চুড়ি বাজিয়ে যাওয়া সুন্দর, না পিঠে বিজ্ঞাপন এঁটে বোবার মতো পায়চারি করা সুন্দর? এদেশে নিরক্ষরতা নেই বলে এদের কানের ক্লেশ কমেছে কিন্তু চোখের জ্বালা? বিজ্ঞাপনওয়ালারা যেন পণ করে বসেছে মানুষের চোখে আঙুল গুঁজে বোঝাবে যে, বিধাতা মানুষকে চোখ দিয়েছেন দোকানদারের ঢাকপেটা চোখ পেতে শুনতে।
লণ্ডনের পথে পথে রথযাত্রার ভিড়, কিন্তু ভিড়ের মধ্যেও শৃঙ্খলা আছে। পুলিশের বন্দোবস্ত অতুলনীয়। কিন্তু কথা হচ্ছে পুলিশের নয়, জনতার—শৃঙ্খলা মেনে চলা যেন এদের দ্বিতীয় প্রকৃতি। রাস্তায় কিছু একটা ঘটেছে, কৌতূহলীরা দাঁড়িয়ে দেখছে, লাইনের পিছনে লাইন; যে লোকটা সকলের শেষে এসে পৌঁছোল সে লোকটা মাত্র দুটো কনুইয়ের জোরে সকলের সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে না, যে আগে এসেছে সে আগে, যে পরে এসেছে সে তার পিছনে কিংবা পাশে। রেলের টিকিট করতে হবে, ঠেলাঠেলি ধস্তাধস্তি ইতর ভাষায় গালাগালি কোনোটাই কোনো কাজে লাগবে না; যে আগে আসবে সে আগে দাঁড়াবে, তার পিছনে তার পরের। ড্রিলের ভাষায় যাকে file বলে কিংবা চলতি ভাষায় যাকে queue বলে তেমনি করে সকলে দাঁড়ালে পরে একজনের পর একজন টিকিট নেবে; সিঁড়ি দিয়ে একে একে ট্রেনের কাছে যাবে, ট্রেনের থেকে যাদের নামবার কথা তারা নামলে পরে ট্রেনে যাদের ওঠবার কথা তারা উঠবে এবং জায়গা থাকে তো আগে মেয়েরা বসবে, না থাকে তো যারা আগে থেকে বসে আসছে তারা উঠে মেয়েদের জায়গা দিয়ে নিজেরা দাঁড়াবে। এইটুকু করতে আমাদের দেশে হাত-পা মুখ-কান সব ক-টা অঙ্গের কসরত হয়ে যায়, বিশেষ করে কানের। এদেশের কিন্তু সমস্ত নিঃশব্দে সারা হয়। ট্রেনে চড়ে হনুমানজির ভজন কিংবা পটলার মার পুরাবৃত্ত শুনে বধির হতে হয় না। কিন্তু এদের এই নিঃশব্দ প্রকৃতি আমার নিছক ভালো লাগেনি। ট্রেনে পাশাপাশি বসতে-না-বসতেই দেশের কেউ গায়ে পড়ে পিতৃপিতামহের নাম শুধায় না। বিয়ে হয়েছে কি না, ক-টি ছেলেমেয়ে, কত মাইনে, কত উপরি পাওনা ইত্যাদি খুঁটিয়ে জেরা করে উত্যক্ত করে না। কিন্তু ওই অনাহূত উপদ্রবের মধ্যে মানুষের ওপরে মানুষের একটা স্বাভাবিক দাবি থাকে—অন্তরঙ্গতার দাবি, সামাজিকতার দাবি; মানুষ যে সমাজপ্রিয় জীব। এদেশের লোকও ও-দাবি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারে না, কিন্তু ওর সঙ্গে কিছু মৌখিকতার খাদ মিশিয়ে দেয়। ‘আজ দিনটা বড়ো ঠাণ্ডা, না?’ ‘তা ঠাণ্ডাই বটে।’ এমনি করে আলাপ আরম্ভ হয়, কিন্তু বেশি দূর এগোয় না, কারণ কথাবার্তার পুঁজিই হল ওয়েদার, পুঁজি ফুরোলে নিঃশব্দে সিগরেট ভস্ম করা ছাড়া অন্য পন্থা থাকে না। এরা বাচাল নয় বটে, কিন্তু বাকপটুও নয়। কথোপকথনের আর্ট এদের অজানা।
বলেছি লণ্ডন শহরে নতুন কিছু দেখবার নেই, আয়তন সমৃদ্ধি ও সজ্জা ব্যতীত। তবু মোটা গোছের গোটা কয়েক প্রভেদ স্থূলদৃষ্টি এড়ায় না। এই যেমন মাটির নীচে টিউব বা ইলেকট্রিক রেলরাস্তা—যেন পাতালপুরীর রাজপথ। যাত্রীরা নীচে নামছে, মিনিটে মিনিটে ট্রেন পাচ্ছে, মাইলের পর মাইল যাচ্ছে, ট্রেন থেকে মাটির ওপরে উঠে আপিস আদালত করছে। মাটির নীচে রেল, মাটির ওপরে ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি। কিংবা যেমন কলে পয়সা ফেললে সিগরেট চকোলেট সর্দি-কাশির ট্যাবলেট থেকে আরম্ভ করে রেলের টিকিট, ডাকঘরের স্ট্যাম্প, স্নানের জল, উনুনের আগুন পর্যন্ত আপনা-আপনি হাজির হয় যেন দেবতাদের বাহন, স্মরণমাত্র উপস্থিত। কিংবা উঁচু-নীচু পাহাড়কাটা রাস্তা, দু-ধারে একই রঙের একই সাইজের এক-এক সারি বাড়ি, একটা দেখলেই একশোটা দেখা হয়ে যায়। বাড়ির আশেপাশে হয়তো এক টুকরো সবুজ, সবুজের ওপরে এক ঝলক রক্ত বা একমুঠো হরিদ্রা। কিংবা যেমন শহরের স্থানে স্থানে মাঠ; গড়ের মাঠের চেয়ে চওড়া তাদের বুক কিন্তু তেমন চিক্বণ নয়, বন্ধুর। মাঠের কোলে কৃত্রিম হ্রদে নরনারী দাঁড় টানে, সাঁতার দেয়, দমদেওয়া পুতুলজাহাজ ভাসায়, হাঁসের সাঁতার দেখে, ছিপ ফেলে মাছের আশায় দিন কাটায়। মাঠের মেঝের ওপরে সবুজ দূর্বার কার্পেট বিছানো, এত সবুজ আর এত প্রচুর যে মুহূর্তকাল অনিমেষ চেয়ে রইলে যেন সবুজ জন্ডিস জন্মায়, তখন যেদিকে চোখ ফিরাই সেদিকে সবুজ। কালো কুৎসিত চিমনির ধোঁয়ায় চোখ যখন নির্জীব হয়ে আসে তখন ওই এক ফোঁটা সবুজ আরক তাকে প্রাণ ফিরিয়ে দেয়।
লণ্ডনের উপবনগুলি নানা জাতের গাছপালায় গহন, গাছেদের মাথায় সোনালি চুল। দুঃখের কথা এ দেশের ফুলে গন্ধ নেই। গুণ নেই রূপ আছে, ফুল নয় তো ফুলবাবু। তাই হাওয়া ফুলের গন্ধে বেহুঁশ হয় না, রাত ফুলের গন্ধে উতলা হয় না, মানুষের একটা ইন্দ্রিয় বুভুক্ষু থেকে যায়। মাঠ বা পার্কগুলি এদের ন্যাশনাল প্লে-গ্রাউণ্ড। সেখানে ছোটো ছেলেরা গাছে ওঠে, ছোটো মেয়েরা বল নাচায়, কিশোরেরা ঘুড়ি ওড়ায়, কিশোরীরা বাজি রেখে দৌড়ায়, যুবক-যুবতীরা টেনিস খেলে, বৃদ্ধেরা বসে বসে ঝিমায়, বৃদ্ধারা কুকুরের শিকল হাতে ঠুকঠুক করে হাঁটে। সেখানে খোকাবাবুরা খুকুমণিরা ঠেলাগাড়িতে চড়ে দিগবিজয়ে বাহির হন, মায়েরা ঠেলতে ঠেলতে চলেন ও চেনামুখ দেখলে ফিক করে হেসে দুটো কথা কয়ে নেন, বাবারা সময় করে উঠতে পারলে খোকা-খুকুর সফরে মায়েদের সহগামী হন, এবং সেখানে যুগলের দল ‘আড়াল বুঝে আঁধার খুঁজে সবার আঁখি এড়ায়।’
মাঠ বা পার্কগুলিতে যতক্ষণ থাকা যায় ততক্ষণ বুঝতেই পারা যায় না যে লণ্ডনের ভিতরে আছি। জনসমুদ্রের মাঝখানে এগুলি এক-একটি দ্বীপ, দ্বীপের চারধারে ঢেউয়ের ওপরে ঢেউ ভেঙে পড়ছে, সেখানে অনন্ত কলরোল। কিন্তু দ্বীপের কেন্দ্রস্থলে তার প্রতিধ্বনি পৌঁছোয় না, তার দুঃস্বপ্ন মিলিয়ে আসে সবুজ আসন পেতে মাটি বলে ‘একটু বসো’ সোনালি চামর দুলিয়ে গাছেরা বলে, ‘একটু জিরিয়ে নাও।’ কিন্তু লণ্ডনের মানুষকে শান্তির মন্ত্রে বশ-মানানো যায় না, দু-দন্ড সে স্থির হয়ে বসতে চায় না, উদ্ভিদের মতো স্থাবর হতে তার আপত্তি, সে জন্ম-যাযাবর। কাজ আর অকাজ তাকে নানান সুরে ডাকে, তার ব্যস্ততার ইয়ত্তা নেই। যেখানে সে আপিস করতে শেয়ার কিনতে টাকা রাখতে যায় সেটার নাম সিটি, প্রায় হাজার দুয়েক বছর আগে তাকে নিয়ে লণ্ডনের পত্তন হয়। সিটির পশ্চিম দিকে ওয়েস্ট এণ্ড। সে অঞ্চলে লোকে বাজার করতে আমোদ করতে আহার করতে যায়। সেখানে বড়ো বড়ো দোকান বড়ো বড়ো হোটেল বড়ো বড়ো ক্লাব বড়ো বড়ো থিয়েটার সিনেমা নাচঘর কনসার্ট হল চিত্রাগার মিউজিয়াম প্রদর্শনী। সিটিতে বড়ো কেউ বাস করে না, ওয়েস্ট এণ্ডে ধনীরা বাস করেন। দরিদ্রের জন্যে ইস্ট এণ্ড আর মধ্যবিত্তদের জন্যে শহরতলিগুলো। এগুলি মোটের ওপর নিরালা স্বাস্থ্যকর ও সুবিন্যস্ত। আমার আক্ষেপ কেবল এই যে, এদের নগরকল্পনায় বিশিষ্টতার স্থান নেই। সবটা জুড়েছে ইউটিলিটি বা প্রয়োজনীয়তা। সুবিধা স্বাচ্ছন্দ্য ও সৌষ্ঠব কার না দরকার? কিন্তু সেই দরকারটাই চরম হল, সৌন্দর্য হল অবান্তর। তাই দেখি প্রশস্ত পরিচ্ছন্ন বাঁধানো পথঘাট, বাতায়নবহুল উপকরণাঢ্য পরিপাটি বাড়িঘর, কিন্তু রাস্তার সব ক-টা বাড়ি একই ধাঁচের, একেবারে হুবহু এক, যেন ছাঁচে ঢালা সিসের টাইপ। এরা সৈনিক নাবিকের জাত কচি বয়স থেকে ড্রিল করতে অভ্যস্ত, সারি বেঁধে গির্জায় যায়, সারি বেঁধে ইস্কুল থেকে ফেরে, এদের চালে চলনে উঠতে-বসতে ড্রিল। তাই এদের ঘরবাড়িগুলো পর্যন্ত লাইন বেঁধে পরস্পরের সঙ্গে সমান ব্যবধান রেখে অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে খাড়া, তাদের সকলের গায়ে ইউনিফর্ম, তার একই মাপ একই রং একই রেখা একই গড়ন। চোখের ক্ষুধায় ক্ষুধার্ত হয়ে তাকাই আর ক্ষোভে নৈরাশ্যে মরিয়া হয়ে উঠি। শুনলুম সমগ্র ইংল্যাণ্ড নাকি সপ্তাহের একই বারে কাপড় কাচতে দেয়, একই বারে কাপড় ফিরে পায়।
শহরের যেকোনো রাস্তায় পা দিলে যে দশটা দোকান সর্বপ্রথম চোখে পড়ে তাদের গোটা দুই মদের দোকান, গোটা দুই রেস্তরাঁ, একটা সিগরেটের, একটা জামাকাপড়ের ও একটা আসবাবের দোকান, একটা খবরের কাগজের স্টল, একটা চুল সাজাবার সেলুন, একটা ব্যাঙ্ক। এর ওপরে যদি টিপ্পনির দরকার হয় তো বলি rum খেয়ে নাকি এরা Somme জিতেছিল, তাই সোমরসের এত আদর। রবিবারেও যে তিনটি দোকান খোলা থাকে তাদের নাম মদের দোকান, সিগরেটের দোকান, খবরের কাগজের স্টল। সিগরেট সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ওর একটা ডিবে কাছে না-থাকলে ভদ্রতা রক্ষা হয় না; কারুর সঙ্গে দেখা হলেই ওটা সামনে ধরে বলতে হয়, ‘নিতে আজ্ঞা হোক।’ এ দেশের মেয়েরা যখন ভালো-মন্দ উভয় বিষয়ে পুরুষের অনুধর্মিণী হবেই বলে কোমর বেঁধেছে তখন তাদের কারোর আলতাপরা মুখে আগুন জ্বলতে দেখলে আশ্চর্য হইনে, কিন্তু কোনো কোনো ভারতবর্ষীয়া যখন স্মার্ট দেখাবার লোভে চিবুকের সঙ্গে সমান্তরাল করে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে সিগরেট লকলক করতে করতে ভুরু কাঁপিয়ে মাথা নাচিয়ে কথা বলেন তখন রিজেন্টস পার্ক চিড়িয়াখানার দৃশ্যবিশেষ মনে পড়ে যায়। দৃশ্যটা আর কিছু নয়, বাঁদরদের টি-পার্টি। মানুষকে ওরা অবিকল নকল করতে পেরেছিল, দুঃখের বিষয় তবু কেউ ওদের মানুষ বলে ভুল করলে না। এদিকে আমি যুবকদের সঙ্গে কথা কয়ে দেখেছি ওরা নিজেরা সিগরেট খায় বলে কুন্ঠিত বোধ করে ও নিজের বোনকে খেতে দেখলে লজ্জিত বোধ করে; কিন্তু পরের বোনকে খেতে দেখলে কেমন বোধ করে এ প্রশ্নটার উত্তরে তাদের মতবিচ্যুতি দেখা গেল। অমন অবস্থায় পড়লে সবারই মত বদলায়।
রেস্তরাঁ যে এ শহরে কত লক্ষ আছে তার গণনা চলে না। আহারের জন্যে রেস্তরাঁ, নিদ্রার জন্যে ফ্ল্যাট বা রুমস—সাধারণ গৃহস্থের জন্যে এই হচ্ছে এখানকার ব্যবস্থা। এ দেশের স্বাচ্ছন্দ্যনীতির সঙ্গে তাল রেখে গৃহস্থালি গড়া বহুসংখ্যক স্ত্রী-পুরুষের পক্ষে দুঃসাধ্য। যাদের সংগতি আছে তারাও বাড়িতে না-খেয়ে বাইরে খায় এই জন্যে যে, সারাদিন যেখানে জীবিকার জন্যে খাটতে হয় বাড়ি সেখান থেকে অনেক দূরে, কিংবা বাড়িতে রান্না করতে যেটুকু সময় লাগে সেটুকুর বাজারদর রেস্তরাঁয় খাবার খরচের চেয়ে বেশি কিংবা বাড়িতে অল্পসংখ্যক লোকের রান্নার যত খরচ রেস্তরাঁয় বহুসংখ্যক লোকের রান্নায় সে অনুপাতে কম। কথা উঠবে তবে বাড়ির মেয়েরা করে কী? তার জবাব এই যে, বাড়ির মেয়েরাও আপিস করে। সকলে নয় অবশ্য, কিন্তু অনেকে। তরুণী মাত্রেই স্কুল কলেজে যায়, বয়স্কা মাত্রেরই কোনো কাজ আছে। মায়েরাও ছেলেদের স্কুলে দিয়ে কাজে যায়, তবে কোলের ছেলে হলে তার গাড়ি ঠেলে মাঠে নিয়ে যায়, খোকা যতক্ষণ হাওয়া খায়, অন্তত ফিডিং বটল চুষে দুধ খায়, খোকার মা ততক্ষণ জামা সেলাই করে। কাজ করে না, বসে খায়, এমন লোক তো দেখছিনে; যার আর কিছু না জোটে সে একটা সভাসমিতি খুলে বসে। সে সব সভাসমিতির উদ্দেশ্যও বিচিত্র; কোনোটার উদ্দেশ্য জবাই করবার অনিষ্ঠুর উপায় উদ্ভাবন, কোনোটার উদ্দেশ্য সদস্যদের মৃতদেহ কবরস্থ না-করে অগ্নিসাৎ করা। ভালো-মন্দ দরকারি অদরকারি কত রকমের অনুষ্ঠান যে এদেশে আছে তার আভাস পাওয়া যায় রবিবারে হাইড পার্কের বেড়ার ভিতর প্রবেশ করলে। একখানা করে চেয়ার জোগাড় করে তার ওপর দাঁড়িয়ে হাত-পা নেড়ে কত বক্তাই যে ভূমিতে দন্ডায়মান বা সম্মুখ দিয়ে চলন্ত শ্রোতৃমন্ডলীকে সম্বোধন করে কত তত্ত্বই প্রচার করেন তার সংখ্যা হয় না। এদেশে ধর্মের হাজারো সম্প্রদায় আছে, রাজনীতির হাজারো দল আছে, বক্তৃতা দেওয়া কাজটাও কঠিন নয়, আর লোকের ভিড়ের ভিতরে এমন দশ-পঁচিশ জন অখন্ড ধৈর্যশীল সহিষ্ণু শ্রোতা বা শ্রোত্রী কি পাওয়া যাবে না যারা অন্তত পঁচিশ মিনিট বিনা পয়সায় গলাবাজি দেখবে বা নাম সংকীর্তন শুনবে? এমনি করেই পাবলিক ওপিনিয়ন সৃষ্ট হয়। শ্রোতারা তর্ক করে, টিটকিরি দেয়, এক বক্তার লোক ভাঙিয়ে নিয়ে আরেক বক্তা উলটো বক্তৃতা শোনায়, তবু সে বক্তার মেজাজ তরুর চেয়ে সহিষ্ণু ও সংকল্প মেরুর মতো অটল; একটিও যদি শ্রোতা না-রয় তবু তার বাক্যের ফোয়ারা ফুরোবে না। হাতে কোনো একটা কাজ না-থাকলে যেন এরা বাঁচতে পারে না, জীবনটা ফাঁকা ঠেকে। চুপ করে বসে থাকা এদের ধাতে সয় না, তাই ছুটি পেলে এরা বড়ো বিব্রত হয়ে ভাবে ছুটি কেমন করে কাটাবে। ভিক্ষা করা এদেশে আইনবিরুদ্ধ; করলে কঠিন সাজা। তাই ভিক্ষুকেরাও কোনো একটা কাজ করবার ভান করে পয়সা রোজগার করে, হয় দু-পয়সার দেশলাই চার পয়সায় বেচে অর্থাৎ বেচবার ভান করে হাত পাতে, নয় ফুটপাথের ওপরে ছবি এঁকে পথিকদের সামনে টুপি খোলে, নয় কিছু একটা বাজিয়ে বা গেয়ে দাতাকে খুশি করে কিন্তু মুখ ফুটে বলে না যে ভিক্ষা দাও, বললেই পুলিশে ধরে নিয়ে যায়। এত কথা এ প্রসঙ্গে বলবার উদ্দেশ্য, এরা কাজ জিনিসটাকে কী চক্ষে দেখে তাই বোঝানো। নিষ্ক্রিয়তাকে এদেশে ধর্ম বলে না।
জামাকাপড়ের দোকানের এত বাহুল্য কেন? একটা কারণ, শীতের দেশের মানুষ কম্বল সম্বল করে ধুনি জ্বালিয়ে নিষ্ক্রিয়ভাবে পরকালের ধ্যান করলে পরকালের দিন ঘনিয়ে আসে, দেহ সম্বন্ধে নির্বিকল্প হলে দেহী মাত্রেই বরফ হয়ে যায়, তাই পথের ভিখারিরও গায়ে ওভার কোট ও পায়ে বুটজুতো চাই। মেয়েরা স্কার্ট হ্রস্ব করে ও গলা খোলা রেখে পরিধেয় সংক্ষেপ করেছে বটে, তবু ওদের পরিধেয় শুধু একখানা শাড়ির মতো সরল নয়। আর একটা কারণ, আংটি বা হার বা দুল ছাড়া অন্য অলংকার বড়ো কেউ পরে না, তাই ভূষণের রিক্ততার ক্ষতিপূরণ করতে হয় বসনের বাহারে। একটু আগে বলেছি এদের নগরস্থাপত্যে বিউটির চেয়ে বড়োকথা ইউটিলিটি। এদের বেশভূষা সম্বন্ধেও ওকথা সমান খাটে। মেয়েরাও এখন কাজের লোক হয়েছে, গজেন্দ্রগমনে চললে ট্রেন ফেল করে আপিস কামাই করে বসবে সেই আশঙ্কায় পক্ষীরাজের মতো মাটি ছুঁয়ে ওড়ে, ছুটে ছুটে হাঁপাতে হাঁপাতে ট্রেনের ওপরে লাফ দিয়ে ওঠে, জায়গা পেলে বসে না-পেলে দাঁড়ায়, এক সেকেণ্ড সময় নষ্ট না-করে খবরের কাগজ কিংবা গল্পের বই বার করে পড়তে আরম্ভ করে দেয়। ছুটোছুটির সুবিধার জন্যে স্কার্টের ঝুল হাঁটুর ওপরে উঠে কোমর অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে। দম আটকাবার ভয়ে গলার ফাঁস খুলতে খুলতে আবক্ষ বিস্তৃত হচ্ছে। স্নান প্রসাধন সুখকর হবে বলে মাথার চুল ছেটে কবরীর অনুপযুক্ত করা হচ্ছে। ফলে শরীর হালকা লাগছে, প্রতি অঙ্গে বাতাস লাগছে, স্বাস্থ্য ভালো থাকছে, স্বাস্থ্যজনিত শ্রীও বাড়ছে; এককথায় স্ত্রীজাতির তথা সমাজের বহুতর উপকার হচ্ছে—ইউটিলিটির দিক থেকে জয়জয়কার। এবং এর দরুন মেয়েরা যে সেক্সলেস বা পুরুষালি হয়ে উঠেছে এমনও নয়। নারীর নারীত্ব যে সাগরতলের চেয়েও অতল; পরিবর্তন সে তো জলপৃষ্ঠের বুদবুদ, কোনো কালেই তা অতলস্পর্শী হতে পারে না; বিপ্লবের মন্দর দিয়ে মথন করেও নারীর নারীত্বকে নড়ানো যায় না, কেবল কাড়তে পারা যায় তার সুধা আর তার বিষ।
পরিবর্তনকে আমি দোষ দিইনে আর ইউটিলিটিকে আমি মহামূল্য মনে করি। তবু আমার ধারণা এ যুগের নারীর পরিচ্ছদ যদি এ যুগের নারীর প্রতিবিম্ব হয় তবে বিম্ব দেখে বলতে পারি বিম্ববতী সুন্দরী নয়। নারীত্বের বিষ যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে সুধাও যাচ্ছে। পরিচ্ছদকে উপলক্ষ্য করে এত কথা বলবার অভিপ্রায়—পরিচ্ছদ তো কেবল নগ্নতার আচ্ছাদন বা শীত বর্ষার বর্ম নয় যে তার প্রয়োজনীয়তাই তার পক্ষে চুড়ান্ত হবে; পরিচ্ছদ যে দেহেরই সম্প্রসারণ, দেহেরই বহির্বিকাশ, দেহের চারপাশে সৌন্দর্যের পরিমন্ডল। এরা জীবনকে ব্যস্ততায় ভরে এমন সংক্ষিপ্ত করে আনছে যে, মানুষের মনের আর সে-অবসর নেই, যে-অবসর নইলে মানুষ নিজের পরিমন্ডল নিজে রচনা করতে পারে না। তখন ডাক পড়ে পোশাক বিক্রেতার আপিসের পোশাক ডিজাইনারকে এবং পোশাক বিক্রেতার দোকানের ম্যানিকিনদের। গণতন্ত্রের বিবেক বন্ধক দেওয়া হয়েছে মন্ত্রীমন্ডলীর কাছে, আর গণতন্ত্রের রুচি বন্ধক দেওয়া হয়েছে লার্জ স্কেল ম্যানুফ্যাকচারওয়ালাদের কাছে। যখন দেখি আজানুলম্বিত আলখাল্লার মতো লোমশ ওভার কোটের অন্তরালে নারীদেহের contour (রেখাভঙ্গি) ঢাকা পড়েছে, দেখা যাচ্ছে কেবল কচ্ছপের খোলার ভিতর থেকে বার করা আজানু উন্মুক্ত পা দুটি আর টুপির দ্বারা রাহুগ্রস্ত মুখটি, তখন মনে হয় যেন দুটি চলন্ত স্তম্ভের ওপরে কালো বা মেটে রঙের একটি বস্তা উপুড় করা হয়েছে; সেই বস্তার পৃষ্ঠভাগ একেবারে প্লেন, তার কোথাও একটা রেখা বা একটা বন্ধনী নেই, কটির স্থিতি যে কোনখানে আর পরিধি যে কতখানি তা অনুমান করে নিতে হয়।
পুরুষের পোশাক সম্বন্ধে কিছু না-বলাই ভালো কারণ পুরুষ চিরকাল কাজের লোক, সে যে ইউটিলিটি ছাড়া অন্য কিছু বোঝে এত বড়ো প্রত্যাশা তার কাছে করা যায় না। মজার কথা এই যে, নারীর পোশাক যত সরল হচ্ছে পুরুষের পোশাক তত জটিল হচ্ছে, তার আপাদমস্তক পোশাক দিয়ে মোড়া; সে-পোশাকের স্তরের পর স্তর, আণ্ডারওয়্যারের ওপরে আণ্ডারওয়্যার, কোটের ওপরে ওভার কোট, জুতোর ওপরে জুতো, মোজার স্পাট, টাই-কলারের ওপরে মাফলার!
শীতের দেশের লোককে বিছানা পুরু করবার জন্যে লেপ কম্বলের বহুল আয়োজন করতে হয়, আর ইউরোপীয় পরিচ্ছদ পরে মেজের ওপরে শোয়া-বসা চলে না বলে খাট পালঙ্ক কৌচ সোফা চেয়ার টেবিল দরকার হয়। এ ছাড়া কাপড় রাখবার ওয়ার্ডরোব, খাবার রাখবার কাবার্ড, হাতমুখ ধোবার সরঞ্জাম, প্রসাধনের আয়না-দেরাজ, রান্নার স্টোভ, ঘর গরম রাখবার অগ্নিস্থলী ইত্যাদি গরিব-দুঃখীরও চাই। দেশে আমাদের বাড়ির ঝি বারান্দায় ছেঁড়া মাদুর পেতে গায়ে ছেঁড়া কম্বল জড়িয়ে শীতের দিনে ঘুঁটের আগুন পোহায়। এখানে আমাদের বাড়ির ঝির জন্যে স্বতন্ত্র ঘর, ঘরের মেজেতে কার্পেট পাতা, দেয়ালে ওয়ালপেপার আঁটা, লোহার খাটে আধ ফুট পুরু বিছানা, ঘরের একপাশে অগ্নিস্থলী, সেখানে কয়লা পোড়াতে হয়, একপাশে টেবিল চেয়ার আয়না দেরাজ আলনা, ওপরে ইলেকট্রিক আলো ও জানালায় নকশাকাটা পর্দা। এই জন্যেই এদেশে আসবাবের দোকান এত। দোকান থেকে আসবাব ভাড়া করে আনতে হয় কিংবা কিনে এনে মাসে মাসে দামের ভগ্নাংশ দিতে হয়। আসবাব সম্বন্ধেও ইউটিলিটির সঙ্গে বিউটির ছাড়াছাড়ি। সৌষ্ঠব আছে কিন্তু বৈশিষ্ট্য নেই, বৈচিত্র্য আছে কিন্তু কলে তৈরি প্রাণহীন বৈচিত্র্য। যন্ত্ররাজ বিভূতির কল্যাণে একালের রামশ্যামও সেকালের রাজরাজড়াদের চেয়ে স্বচ্ছন্দে আছে। কিন্তু রামের সঙ্গে শ্যামের এখন একতিলও তফাত নেই; রামের নাম ৪৬ঙ তো শ্যামের নাম ৪৭ঙ; নামের তফাত নেই, সংখ্যার তফাত। ‘কলি’ যুগ বটে!
আমাদের বাড়ির ঝি ফুরসত পেলেই খবরের কাগজ পড়ে; কোনো কোনো দিন খাবার সময়, কোনো কোনো দিন পরিবেশন করবার ফাঁকে। এই থেকে বুঝতে হয় এদেশে খবরের কাগজের কেমন প্রচার ও প্রভাব। যে কাগজ আমাদের ঝি পড়ে সে কাগজে গুরুগম্ভীর লেখা থাকে না, তার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ আধ কলমও নয়, সম্পাদক মহাশয় হালকা সুরে গ্রেহাউণ্ড রেসিং বা শরৎ কালের ফ্যাশন সম্বন্ধে দু-চার কথা বলে আমাদের ঝি ঠাকরুনের সন্তোষবিধান করেন, উঁচুদরের রাজনৈতিক চাল বা অর্থনৈতিক সমস্যার ধার দিয়েও যান না; সংবাদের কলমে থাকে খেলাধুলা, ঘোড়দৌড়, চোর-ডাকাত, বিবাহ ও বিবাহভঙ্গ ইত্যাদি চটকদার ও টাটকা খবর। আদালতে কে কেঁদেছে, এরোপ্লেনে কে হেসেছে, থিয়েটারে কে নেচেছে তাদের ফোটো তো থাকেই, সময় সময় তাদের সঙ্গে ‘আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি’-র সাক্ষাৎকারের লোমহর্ষণ বিবরণ থাকে। ‘আমাদের দেশের কাগজের সঙ্গে এদেশের কাগজগুলোর মস্ত একটা তফাত এই যে, এদেশের কাগজে গালাগালি থাকে না; ক্যাথরিন মেয়োর ওপর রাগ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু তাকে বেশ্যা বলে গালাগাল দেওয়াটা ইতরতা। অমন ইতরতা এদেশের কাগজওয়ালারা এদের প্রধানতম শত্রুদের বেলাও করে না। পাঞ্চ কাগজখানার পেশাই হচ্ছে ভাঁড়ামি, কিন্তু সে ভাঁড়ামির মধ্যে অশ্লীলতা থাকে না। এদেশে ক্যাথরিন মেয়োর যারা প্রশংসা গেয়েছে তারা স্পষ্ট করে বলতে ভোলেনি যে লেখিকা ইংরেজ নয়, আমেরিকান; এবং অনেকে ইঙ্গিতে বুঝিয়েছে যে, ইংরেজ লেখক হলে কুরুচি-পরিচায়কপ্রসঙ্গগুলো অমন খোলাখুলিভাবে বীরদর্পে উল্লেখ করত না। বাস্তবিক, অশ্লীলতা সম্বন্ধে ইংরেজ জাতির একটা স্বাভাবিক ভীরুতা আছে, তাই এদেশের খবরের কাগজে কেলেঙ্কারির বর্ণনাটাও নীচু গলায় হয়। মোটকথা, রেসপেক্টেবল বলে গণ্য হবার জন্যে এদেশের ‘ইতরেজনা’-র একটা ঝোঁক আছে, তাই ডেলি হেরাল্ডকেও টাইমসের আদর্শ অনুসরণ করতে হয়। আমাদের ঝি ঠাকরুনের শ্রেণির মেয়েরাও মনে মনে এক-একটি লেডি। ইংল্যাণ্ডের গণতন্ত্রে অভিজাতদের ক্ষমতা কমেছে, কিন্তু প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে, অর্থাৎ এদেশ কুলীনকে অন্ত্যজ না-করে অন্ত্যজকে কুলীন করে তুলছে।
এর পরের প্রসঙ্গ, চুল সাজাবার সেলুন। এই জিনিসটা আগে এদেশে পুরুষদের জন্যে অভিপ্রেত ছিল, সুতরাং সংখ্যায় অর্ধেক ছিল। এখন মেয়েরা হয় পুরুষের মতো ছোটো করে চুল ছাঁটে, নয় হরেক রকমের বাবরি রাখে। শিংল করাটা একটা আর্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে, এ আর্টের আর্টিস্ট হচ্ছেন নরসুন্দর আর তুলি হচ্ছে তাঁর কাঁচি। যার চুল যেমন করে শিংল করলে মানায় তার চুল তেমনি করে শিংল করাটা যথেষ্ট সৌন্দর্যবোধের পরিচায়ক। তবে ব্যাপারটা ব্যয়সাধ্য, মাসে মাসে নরসুন্দরকে খাজনা গুনতে হয়। চুল ছেঁটে নাকি মেয়েরা সোয়াস্তি পায়। সম্ভবত পায়, কিন্তু এক্ষেত্রেও সেই ইউটিলিটির প্রশ্ন। আগে ইউটিলিটি, তারপরে ওরই ওপরে একটু সৌষ্ঠবের ব্যবস্থা, সেজন্যে নরসুন্দরের শরণাপন্ন হওয়া। নিজের রুচি পরের কাছে বন্ধক রাখা ও শতসংখ্যকের জন্যে লার্জ স্কেলে সৌন্দর্য ম্যানুফ্যাকচার করা। ভবিষ্যতে নরসুন্দরের কুটিরশিল্পটা বিদ্যুৎচালিত কারখানাশিল্পে পরিণত হবে না তো? সুন্দরীরা দলে দলে কলের নীচে মাথা পেতে slot-এ ছ-পেনি ফেললে আপনা-আপনি চুল ছাটা টেড়ি কাটা ঢেউ-খেলানো শিং-বাঁকানো কান-ঢাকানো কলপ-মাখানো পাঁচ মিনিটে সমাপ্ত হবে না তো?
এবার ব্যাঙ্কের কথা বলে আজকের মতো পাততাড়ি গুটাই। সকল বাবুয়ানা সত্ত্বেও ইংরেজরা হিসাবি জাত, যেমন ফুর্তি করে তেমনি খাটে এবং খাটুনির অর্জন থেকে যতটা ব্যয় করে ততটার বহুগুণ সঞ্চয় করে। ব্যাঙ্ক হচ্ছে প্রত্যেকের খাজাঞ্চিখানা। ঘরে টাকা না-রেখে সেইখানে গছিয়ে দেয় ও দরকার হলেই চেক লিখে দেয়। আমাদের বাড়ির ঝিও ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেয়, সে-টাকা দেশের ব্যবসাবাণিজ্যে খাটে, তার থেকে সে সুদ পায়। ইংল্যাণ্ডে অগণ্য ব্যাঙ্ক আছে, পাড়ায় পাড়ায় ব্যাঙ্কের শাখা। পাড়ায় ওই ব্যাঙ্কটি না থাকলে পাড়ায় ওই ন-টি দোকানও থাকত না, এ সমৃদ্ধিও থাকত না। আমাদের বাড়ির ঝি টাকা না জমিয়ে উড়িয়ে দিত কিংবা মাটিতে পুঁতে টাকার ব্যবহারই করত না। ব্যাঙ্ক থাকায় আমাদের বাড়ির ঝির দশ-বিশ টাকা পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরছে, এই মুহূর্তে হয়তো নিউজিল্যাণ্ডের চাষারা ওই টাকা ধার নিলে, কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকার সোনার খনির মালিকেরা ওই টাকার সুদ দিলে, কিংবা হাওড়ার পাটের কলওয়ালারা ওই টাকার শেয়ারে ওর দু-গুণ ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করলে।
৩
নতুন দেশে এলে মানুষের সব ক-টা ইন্দ্রিয় একসঙ্গে এমন সচেতন হয়ে ওঠে যে, মিষ্টান্নের দোকানে শিশুর মতো মানুষ কেবলই উতলা হয়ে ভাবে কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখি, কোনটা ছেড়ে কোনটা শুনি, কোনটা রেখে কোনটা নিই। একান্ত তুচ্ছ যে, সেও নবীনত্বের রসে ডুব দিয়ে রূপকথার দাসীকন্যার মতো রানির যৌবন নিয়ে সম্মুখে দাঁড়ায়। বলে, দ্যাখো দ্যাখো আমাকে দ্যাখো, আমি ভালো নই মন্দ নই, সুন্দর নই কুৎসিত নই, আমি রূপবান আমি নতুন। তখন মানুষের ভিতরকার রসিকটি দেহ-দুর্গের চার দেয়ালের দশ জানালা খুলে দিয়ে জানালার ধারে বসে। সে নীতিনিপুণ নয়, সে ভালো-মন্দ ভাগ করে ওজন করে বিচার করতে পারে না, সে কেবল দেখতে শুনতে চাখতে ছুঁতে চায়; কিন্তু কত দেখবে, কত শুনবে, কত চাখবে, কত ছোঁবে! হায়, আমার যদি সহস্রটা চোখ সহস্রটা কান থাকত, আর থাকত সহস্রটা—না না, পাঁচশোটা মন, তাহলে জগতের আনন্দ-যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ এমন ব্যর্থ যেত না। তাহলে আমি হাল ছেড়ে দিয়ে ঘরের কোণে বাতির নীচে আগুনের দিকে পিঠ করে বসে বিচিত্রা-র জন্য ভ্রমণকাহিনি লিখতুম না, আমি আর এক বিচিত্রার দ্যুলোক-ভূলোকব্যাপী অফুরন্ত লীলা উপভোগ করতে পথে বেরিয়ে পড়তুম। কিন্তু দ্যুলোকব্যাপী?—হায়, লণ্ডনের কি দ্যুলোক আছে! লণ্ডনের লঙ্কাপুরীতে ভুবনের ঐশ্বর্য আহৃত, কিন্তু আকাশ নেই, সূর্য নেই, চন্দ্র নেই, তারা নেই। দিনের পর দিন যায়, সূর্য ওঠে না, আকাশ মানিনীর মতো মুখ আঁধার করে রাখে, আর আমরা নিরীহ লণ্ডনবাসীরা পিতামাতার দ্বন্দ্বে অবোধ শিশুর মতো অবহেলিত হয়ে আলোর ক্ষুধায় অতিষ্ঠ হই। আমাদের জ্যেষ্ঠরা যাঁরা লণ্ডনের কোলে দীর্ঘকাল আছেন তাঁরা হিন্দু বিধবার মতো উপবাস সইতে অভ্যস্ত কিন্তু আমরা কনিষ্ঠরা আলোর দেশ থেকে সদ্য আগন্তুক, ডাল-ভাতের বদলে মাংস-রুটি খেয়ে দেহধারণ করতে যদিচ পারি, তবু সূর্যের আলোর অভাবে গ্যাসের আলো ছুঁইয়ে মনের বৃন্তে ফুল ধরাতে পারিনে। শুনেছি রবীন্দ্রনাথ ইউরোপে এলে, শ্রীকৃষ্ণ বিয়োগে অর্জুন যেমন গান্ডিব তুলতে অক্ষম হয়েছিলেন, রবির বিরহে কবিতা লিখতে তেমনি অক্ষম হন। আলোর দেশের মানুষের দেহ আলোর সঙ্গে ছন্দ রেখে গড়া, তার লোমকূপে-কূপে আলোর আকাঙ্ক্ষা জঠরজ্বালার মতোই সত্য। সেই দেহের ওপরে যখন সপ্তাহের পর সপ্তাহ অনবচ্ছিন্ন অন্ধকারের চাপ পড়ে তখন মন বেশিদিন অস্বস্তির ছোঁয়াচ এড়াতে পারে না, সূর্যাস্তের পরে তরুর মতো মাথা যেন নিস্তেজ হয়ে নুয়ে পড়ে।
এক একদিন কালো কুয়াশায় দিনের ভিতর রাতের জের চলে, রাতের দুঃস্বপ্ন যেন বুকের ওপরে বসে ক্ষান্ত হয় না, দিনের বেলা মনেরও ওপরে চাপে। এক-একদিন সাদা কুয়াশায় সামনের মানুষ দেখা যায় না, পদাতিকের দল ‘চলি-চলি-পা-পা’ করে শিশুর মতো হাঁটে, মোটর গাড়িতে ঘোড়ার গাড়িতে মন্থরতার প্রতিযোগিতা বাঁধে, তবু তো শুনি গাড়িতে গাড়িতে মাথা ফাটাফাটি হয়, পথের মানুষ গাড়ি চাপা পড়ে মরে। হঠাৎ এক এক দিন মেঘ-ধোঁয়া-কুয়াশার পর্দা তুলে আকাশের অন্তঃপুরে সূর্যের পদপাত হয়, আমাদের মুখের ওপরে খুশির হাসির লহর খেলে যায়। দু-তিন সপ্তাহে একদিন করে আলোর জোয়ার আসে, দু-এক ঘণ্টায় তার ভাটা পড়ে, তবু সেই দুটি-একটি ঘণ্টার জন্যে আমরা সমরখন্দ ও বোখারা দান করতে রাজি আছি। এক সহস্র ক্যাণ্ডল-পাওয়ার-বিশিষ্ট বিজলির আলোর চেয়ে এক কণা সূর্যের আলোর দাম যে কত বেশি তা যেদিন নয়নঙ্গম হয়, সেদিন—
না চাহিতে মোরে যা করেছ দান
আকাশ আলোক তনু মন প্রাণ
সে মহাদানের মূল্য হৃদয়ঙ্গম করে লণ্ডনের বিভবসম্ভোগ তুচ্ছ মনে হয়। দৈবাৎ এক-আধ বার চাঁদ দেখা দেয়। আমার বিরহী বন্ধুটি খবর দিয়ে যায় চাঁদ উঠেছে—সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে আসা চাঁদ, কোনো বিরহিণীর পাঠিয়ে দেওয়া চাঁদ। আমাদের কাছে চাঁদের মতো আশ্চর্য আর নেই; সে তো কেবল আলো দেয় না, সে দেয় সুধা। বিজলির আলোর সঙ্গে তার তফাত ওইখানে। সভ্যতা আমাদের কেরোসিনের আলোর পরে গ্যাসের ও গ্যাসের আলোর পরে বিজলির আলো দিয়ে অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে চলেছে, কিন্তু প্রকৃতি আমাদের দয়া করে যে সুধাটুকু দিয়েছে সভ্যতা তার পরিমাণ বাড়াতে পারেনি।
কথা হচ্ছিল নতুন দেশে এলে মানুষের সব ক-টা ইন্দ্রিয় একসঙ্গে এমন সচেতন হয়ে ওঠে যে, মানুষের দশা হয় সেই ভদ্রলোকের মতো যে-ভদ্রলোক একপাল আত্মীয় পরিবৃত হয়ে কাশীতে বা পুরীতে ট্রেন থেকে নামেন। দশটা পান্ডা যখন দশটি আত্মীয়কে ছিনিয়ে নিয়ে দশ দিকে রওনা হয় এবং আরও দশটা এসে কর্তার দশ অঙ্গে টান মারে, তখন তাঁর যে অবস্থা হয় আমার মনেরও এখন সেই অবস্থা। ঘর ছেড়ে একবার যদি বার হই তো লণ্ডন শহরের সব ক-টা রাস্তা একসঙ্গে আহ্বান করতে থাকবে—‘এদিকে, বন্ধু, এদিকে’, সব ক-টা মাঠ উদ্যান, সব ক-টা মিউজিয়াম, আর্ট গ্যালারি, থিয়েটার, কনসার্ট সমবেত স্বরে গান করে উঠবে—‘এখানে বন্ধু, এখানে।’ তাদের আহ্বান যদি না-ই শুনি, যদি কোনো একটা রাস্তা ধরে খ্যাপার মতো যেদিকে খুশি পা চালাই, তবে মানব-মানবীর শোভাযাত্রা থেকে কত রঙের পোশাক, কত ভঙ্গির সাজ, কত রাজ্যের ফুলের মতো মুখ আমার চোখ দুটিকে এমন ইঙ্গিতে ডাকবে যে, মনটা হাল ছেড়ে দিয়ে ভাববে, এর চেয়ে চুপ করে ঘরে বসে ভ্রমণকাহিনি লেখা ভালো, বৈরাগ্যবিলাসীর মতো সমস্ত ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ করে সর্ব প্রলোভনের অতীত হওয়া ভালো, সুরদাসের মতো দুটি চক্ষু বিদ্ধ করে ভুবনমোহিনী মায়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া ভালো।
আমি ঘরে বসে লিখছি, আমার চোখজোড়া অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো ভূপ্রদক্ষিণে বেরিয়েছে। প্রথমে যেখানে গেল সেটা আমাদের বাড়ির পাশের টেনিস কোর্ট, সেখানে যুবক-যুবতীরা লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে ছুটে হেসে হেসে খেলছে। যে দুটো জাতির পরস্পরের থেকে শতহস্ত ব্যবধানে থাকা উচিত, সেই দুটো জাতি যে বয়সে মানুষের শিরায় শিরায় ভোগবতীর বন্যা ছোটে সেই বয়সে কেবল যে স্বাস্থ্যের জন্যে শীতবাতাসের মধ্যে আঁধার আকাশের তলে খেলা করছে তা নয়, সেইসঙ্গে এত প্রচুর হাসছে যে ভারতবর্ষের লোক মোহমুদগরের আমল থেকে আজ অবধি সব মিলিয়ে এত হাসেনি। আমার চোখ ঘরের জানলা ছেড়ে রাস্তায় নামল। আমাদের পাড়ার বাড়িগুলো এক পায়ে দাঁড়িয়ে-থাকা ঘুমন্ত বকের মতো নিস্তব্ধ। এটা একটা শহরতলি। সামনের বাড়ির ঝি মাটিতে হাঁটু গেড়ে কোমরে কাপড় জড়িয়ে সিঁড়ির ওপর ন্যাতা বুলোচ্ছে, তার হাত প্রতি দেশের কল্যাণী নারীর হাত, ধুলা যার স্পর্শ পেয়ে প্রত্যহ শুচি হয়। আমার চোখ এগিয়ে চলল। এরপরের রাস্তাটা পাহাড় থেকে নেমেছে, তার নামবার মুখে খাস লণ্ডন। নামতে নামতে দেখছি ছেলের দল পায়ে চাকা বেঁধে ফুটপাথের ওপর দিয়ে সোঁ করে নেমে চলেছে, চলতে চলতে বাঁধালো হয়তো কোনো বুড়ো ভদ্রলোকের গায়ে ধাক্কা, বার্ধক্যের চোখ তারুণ্যের দিকে কোমল ভাবে চাইল। ছোটো মেয়েরা দোকানের কাচের বাইরে থেকে ভিতরের কেক চকোলেটের দিকে লুব্ধ নিরাশ দৃষ্টি ফেলছে; হয়তো দার্শনিকের মতো ভাবছে, কমল যদি এত সুন্দর তো কমলে কণ্টক কেন? চকোলেট যদি এত সুস্বাদ তো চকোলেটের চারপাশে কাচের বেড়া কেন? আমার চোখ পথে চলতে চলতে দেখছে মদের দোকানের ওপর বিজ্ঞাপনের নামাবলি, গির্জার দ্বারদেশে মুদ্রিত ধর্মানুশাসন, কসাইয়ের দোকানে দোদুল্যমান হৃতচর্ম পশুর শব, কেমিস্টের দোকানে নানা রোগের দাওয়াই, পোশাকের দোকানের কাচের এক পারে হঠাৎ থামা নারীর কৌতূহলদৃষ্টি, অন্য পারে চোখ-ভুলানো পোশাকের নমুনা ও দাম। ফলের দোকানের কর্মচারিণী বাইরের কাচ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করছে। ‘এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সি’-র কর্ত্রী ঝিদের জন্যে গিন্নি ও গিন্নিদের জন্যে ঝি ঠিক করে দিচ্ছেন। সরকারি ইস্কুলের এক প্রান্তে ছেলেরা ও অপর প্রান্তে মেয়েরা সমান বিক্রমে মাতামাতি করছে; তাদের ভাগ্য ভালো, ভারতবর্ষে জন্মায়নি; সে দেশে জন্মালে এতদিনে ছেলেরা গোপাল হয়ে উঠত, মেয়েরা মেয়ের মা হত।
আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেলস্টেশনের কাছে এসে আমার চোখ দোটানায় পড়েছে—ট্রেনে চড়বে না বাসে উঠবে? বাসেই উঠল, দোতলার এককোণে আসন নিল। দু-পাশে দোকান-বাজার, দোকানে ক্রেতা-ক্রেত্রীর ভিড়, কর্মচারিণীদের ব্যস্ততা; উভয় পক্ষে শিষ্টাচার। রেস্তরাঁ—দলে দলে নরনারী আহারে রত; পরিবেশনকারিণীদের মরবার ফুরসত নেই, ছুরি-কাঁটা-প্লেটের ঝনৎকার; সুখভোগ্য খাদ্যপেয়ের সুগন্ধবাহী ধোঁয়া। রেস্তরাঁর বাইরে অন্ধ ভিক্ষুক চীরধারিণী পত্নীর হাত ধরে দেশলাই বেচছে বা বাজনা বাজাচ্ছে বা ফুটপাথে ছবি আঁকছে। রাস্তা মেরামত করছে কুলিরা, তাদের পরিধান কাদামাখা ও জীর্ণ, মুখে প্রতি দেশের কুলি-মজুরের মতো সরলতাব্যঞ্জক প্রাণখোলা হাসি। জমকালো পোশাকপরা অশ্বারোহী সৈনিক চলেছে, বুড়িরা হাই তুলতে তুলতে নির্নিমেষে দেখছে। গত যুদ্ধে তাদের এমনি-সব ছেলেরা তো মরেছে! তরুণীরা গৃহবাতায়ন থেকে উল্লাসধ্বনি করছে, যৌবন যে ঠেকেও শেখে না, হারিয়েও হারায় না। থিয়েটারের ম্যাটিনির সময় হল, টিকিট কেনবার জন্যে স্ত্রী-পুরুষ ‘কিউ’ (queue) করে দাঁড়িয়েছে, দুজনের পেছনে দুজন—পুরুষের চেয়ে স্ত্রী সংখ্যা বেশি। সর্বত্র পুরুষের চেয়ে স্ত্রী সংখ্যা বেশি—সভাসমিতিতে স্কুলে কলেজে থিয়েটার কনসার্টে দোকানে আপিসে সর্বত্র নারীর আক্রমণে পুরুষ পলাতক। কেরানি মানে নারী, স্কুলশিক্ষক মানে নারী, গৃহভৃত্য মানে নারী। রাস্তার মোড়ে বাস থামল, শালপ্রাংশু বলিষ্ঠকায় পুলিশের তর্জনী সংকেতে শত শত বাষ্পীয় যান থেমেছে, শতশত নরনারী রাস্তা পারাপার করছে। মেয়েরা ধাক্কা দিতে দিতে ধাক্কা খেতে খেতে ভিড়ের মধ্যে ছুটে মিলিয়ে যাচ্ছে ছটকে বেরিয়ে পড়ছে। শিশু কাঁখে নিয়ে শিশুর বাবা তার মা-র পশ্চাদবর্তী হচ্ছেন। বুড়িকে ঠেলাগাড়িতে বসিয়ে বুড়ির ছেলেমেয়েরা মাঠে হাওয়া খাওয়াতে যাচ্ছে। প্রেমিক যুগল হাতে হাত জড়িয়ে বাজার করে ফিরছেন। বাস চলতে আরম্ভ করল, একটা পার্কের কাছ দিয়ে যাচ্ছে, পার্কের বেঞ্চিতে বসে কাগজ পড়তে পড়তে দরিদ্ররা রুটি কামড়ে খাচ্ছে—তাদের মধ্যাহ্নভোজনটা দু-একখানা রুটিতেই সমাপ্ত হচ্ছে।
বাস কলেজের কাছে থামতেই আমার চোখজোড়া তৎক্ষণাৎ নেমে পড়ে দৌড় দিলে কলেজের অভিমুখে। কোনো অগ্রগামিনী হয়তো দয়া করে দরজাটা খুলে রাখলেন, প্রবেশ করে ধন্যবাদ দিয়ে কপাটটা খুলে ধরা গেল পশ্চাদাগতের জন্যে। তারপর ক্লাসে গিয়ে আসন অধিকার করা; অধ্যাপকের আগমনের আগে মেয়েদের তুমুল ফিসফাস; কে কী সাজ করে এসেছে অন্যমনস্কতার ভান করে দেখা ও দেখানো লাফ দিয়ে পেছনের চেয়ার থেকে সামনের চেয়ারে যাওয়া; অধ্যাপকের প্রবেশ; অধ্যাপকোবাচ—সুবোধ বালিকাদের কর্তৃক একান্ত তন্ময়ভাবে তাঁর প্রত্যেকটি কথার শ্রুতিলিখন; পলাতকমতি উন্মনা বালক কর্তৃক উপন্যাস পাঠ বা কবিতাসংরচন; বার বার ঘড়ির দিকে চাতক দৃষ্টিক্ষেপ; অবশেষে ছাত্র-ছাত্রীদের ছত্রভঙ্গ; ধাক্কাধাক্কিপূর্বক ক্লাস থেকে বহির্গম।
নতুন দেশে এলে কেবল যে সব ক-টা ইন্দ্রিয় সহসা চঞ্চল হয়ে ওঠে তা নয়, সমস্ত মনটা নিজের অজ্ঞাতসারে খোলস ছাড়তে ছাড়তে কখন যে নতুন হয়ে ওঠে তা দেশে ফিরে গেলে দেশের লোকের চোখে খট করে বাঁধে, নিজের চোখে ধরা পড়ে না। মানুষ খাদ্য পেয় সম্বন্ধে বোধ হয় কিছু রক্ষণশীল, দেশি রান্নার স্বাদ পেলে রসনা আর কিছু চায় না। কাঁচা বাঁধাকপি চিবিয়ে খেতে যতখানি উৎসাহ দরকার, বাঁধাকপির ডালনাচোখা রসনা কোনো জন্মে ততখানি উৎসাহ সংগ্রহ করতে পারে না। কিন্তু পরিচ্ছদ সম্বন্ধে মানুষের এতটা রক্ষণশীলতা নেই। দেশে যখন এক-আধ দিন কোট-ট্রাউজার্স পরা যেত সে কী অস্বস্তি আর সে কী সাহেব মানসিকতা! ধুতি-পাঞ্জাবিপরা বাঙালিগুলোর ওপরে তখন কী অকারণ করুণা! জাহাজে থাকবার সময় জাহাজি কানুনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ধুতি-পাঞ্জাবি পরার স্মৃতি মনে পড়ে গেলে হাসি পায়। এতদিনে ইউরোপীয় ধড়াচূড়া গায়ে বসে গেছে, চব্বিশ ঘণ্টা এই বেশে থাকতে একটুও বেখাপ্পা বোধ হয় না; এখন মনে হয় এইটেই স্বাভাবিক, যেন এই পোশাক পরে ভূমিষ্ঠ হয়েছি। প্রতিদিন যন্ত্রচালিতের মতো টাইটা বাঁধি, ট্রাউজার্স জোড়াটার হাঁ-দুটোতে পা জোড়াটা গলিয়ে দিই, মন খানেক ভারী ওভারকোটটার বাহন হয়ে চলি। দৈবাৎ কোনোদিন ধুতি পাঞ্জাবি চাদর বার করে পরি তো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারিনে; আমোদের অন্ত থাকে না, জগৎকে দেখিয়ে আসতে ইচ্ছা করে আমাদেরও জাতীয় পরিচ্ছদ আছে। কিন্তু আমাদের জাতীয় পরিচ্ছদ কি একটা? মাদ্রাজি ভায়াদের সঙ্গে পাঞ্জাবি ভায়াদের আপাদমস্তক অমিল, বাঙালি মুসলমান পেশোয়ারি পাঠানের যমজ ভ্রাতা নন। আমার সফেদ ধুতি আর সবুজ পাঞ্জাবিটার ওপরে নীলকৃষ্ণ উত্তরীয়খানা জড়িয়ে ঘরের বাইরে পা বাড়াই তো রাস্তায় ভিড় জমে যাবে; পুলিশ যদি-বা আমাকে মানুষ বলে চিনতে পেরে চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষদের হাতে সমর্পণ না-করে তো ট্রাফিক বন্ধ করার অজুহাতে সর্বজনীন শ্বশুরালয়ে চালান দেবে।
নতুন দেশে এলে নতুন আবহাওয়ায় নিশ্বাস নিয়ে গোটা মানুষটারই একটা অন্তঃপরিবর্তন ঘটে যায়। যাঁরা বলেন তাঁদের পরিবর্তন হয়নি তাঁরা খুব সম্ভব জানেন না কোথায় কী ঘটে গেছে। দেশে ফেরবার সময় তাঁরা সর্বাংশে, এমনকী মতবাদেও, ঠিক সেই মানুষটি থেকেই ফিরতে পারেন; কিন্তু মনেরও অগোচরে মানুষের কোনখানে কোন প্যাঁচটি আলগা হয়ে যায় তা মানুষ কোনোদিন না জানতে পারলেও সত্যের নিয়ম অমোঘ। নিজেকে জেরা করলে বুঝতে পারি দেশে ফিরে গেলে আমার যেন সেই অবস্থা হবে যে অবস্থা হয় দিঘিতে ফিরে গেলে স্রোতের মাছের। ইউরোপের জীবনে যেন বন্যার উদ্দাম গতি সর্বাঙ্গে অনুভব করতে পাই। ভাবকর্মের শতমুখী প্রবাহ মানুষকে ঘাটে ভিড়তে দিচ্ছে না, এক-একটা শতাব্দীকে এক-একটা দিনের মতো ছোটো করে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সবচেয়ে স্বাভাবিক বোধ হচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদিনের প্রতি কাজে সংযুক্ত থেকে নারী ও নরের একস্রোতে ভাসা। নারী সম্বন্ধে এদেশের পুরুষ দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা নিয়ে মুমূর্ষুর মতো বাঁচে না, নারীর মাধুর্য তার দেহকে ও মনকে তুল্যরূপ সক্রিয় করে তোলে। কেবল চোখে দেখারও একটা সুফল আছে, মানুষের রূপবোধকে তা ঐশ্বর্যান্বিত করে দেয়। নারীকে অবরুদ্ধ রেখে আমাদের দেশের পুরুষ নিজের চোখের জ্যোতিকে নিজের হাতে নিভিয়েছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে অন্য কোনোবার লিখব। যা আমার কাছে তর্ক নয়, রহস্য নয়, সহজ অনুভূতি, তাই আমাদের দেশের লোকের কাছে বাক্যের সাহায্যে বোঝাতে হবে—দুর্ভাগ্য! বেশ বুঝতে পারি দেশে ফিরে গেলে দেশটা পার্টিশন দেওয়া ঘরের মতো ঠেকবে—একপাশে পুরুষ একপাশে নারী মাঝখানে সহস্র বৎসরের অন্ধ সংস্কার।
আর একটা সহজ অনুভূতি, মানুষের সঙ্গে মানুষের সমস্কন্ধের মতো মেশা, কোনো ব্রাহ্মণের কাছে নতশির থাকতে হয় না, কোনো দারোগার কাছে বুকের স্পন্দন গুনে চলতে হয় না, কোনো মনিবের কাছে মাটিতে মিশিয়ে যেতে হয় না, মনুষ্যমর্যাদাগর্বে প্রত্যেকটি মানুষ গর্বিত। ভারতবর্ষের মাটিতে পা দিলে এই মুক্ত মানসিকতার অভাব সমস্ত মন দিয়ে বোধ করব। ভারতবর্ষ যে প্রভু-মানসিকতার দেশ, দাস-মানসিকতার দেশ, সেখানে প্রত্যেকটি মানুষ একজনের দাস অন্য জনের প্রভু।
৪
বড়োদিনের ছুটিতে লণ্ডন ছেড়ে লেজাঁয় গিয়ে দেখি, সে এক তুষারময় স্বপ্ন, যেন নিসর্গের তাজমহল। নিবিড় নীল অকূল আকাশে সেটি একটি পর্বতদিগবলয়িত নিরালা তুষারদ্বীপ; তার মাটি বরফের, মেঘ বরফের; তার জল-স্থল-অন্তরিক্ষের ভিত দেয়াল ছাদ মর্মরনিভ বরফের। যেন আকাশসিন্ধুর ঢেউয়ের পর ঢেউ পাহাড়ের পর পাহাড় হয়ে উঠেছে আর ফেনায় ফেনায় মাটির বেলা ঢেকে গেছে। সে আকাশ এতই নীল আর এত উজ্জ্বল আর এত সুন্দর যে চাতকের মতো দিবারাত্র অনিমেষ চেয়ে থেকে সাধ মেটে না, মনে হয় এ এক মহার্ঘ বিলাসিতা, শুধু এরই জন্যে এক সমুদ্র একাধিক নদী পেরিয়ে ফ্রান্সের এক সীমানা থেকে আরেক সীমানা অবধি রেলদৌড় দিয়ে সুইস আল্পসের শাখাশিখরে উঠতে হয়। সে তো লণ্ডনের মাথার ওপরে কালো শামিয়ানার মতো খাটানো দশ হাত উঁচু দশ হাত চওড়া দশ হাত লম্বা আকাশ নয় যে চোখ বাড়ালেই নাগাল পাব, মন বাড়ালেই মাথা ঠুকে মরব, দশ দিকের পেষণে ধৃতনিশ্বাস হব। লেজাঁয় যেদিন নামলুম সেদিন অসহ আনন্দে নিজেকে শতধা করতে পারলে বাঁচতুম। মুক্ত আকাশের মধ্যে মানবাত্মার যে মুক্তি সে মুক্তি আর কিছুরই মধ্যে নেই। সেই আকাশকে যারা কয়লার ধোঁয়া দিয়ে কালো করে দশ-তলা বাড়ির ঘের দিয়ে খাটো করে তুলেছে তারা কুবের হলেও কৃপার পাত্র, তারা স্বখাদ-সুড়ঙ্গতলের যখ।
সেই উজ্জ্বল নীল প্রশস্তপরিধি আকাশে যখন এক পাহাড়ের ওপার থেকে সূর্য উঠি-উঠি করে, মেঘের মুখে সেই সংবাদ পেয়ে আর পাহাড়ের এপারের বরফ হিরের মতো ঝকমক করে, রঙের সপ্তকের ওপর আলোর আঙুল ঝলমল ঝিলমিল করে পিয়ানোর ঝংকার তুলে যায়, তখন মুহূর্তের জন্য অনুভব করতে পারি আদিযুগের ধ্যানীর চেতনায় কেমন জ্যোতি ঝলসে উঠেছিল, কোন আবিষ্কারের অসম্বরা বাণী তাঁর কন্ঠভেদ করে আপনি ফুটেছিল, কীসের আনন্দে তাঁকে বলিয়েছিল :
শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ
বেদহং মেত পুরুষং মহান্তম আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
সারাদিন সূর্যকিরণ ছোঁয়াতে ছোঁয়াতে চলে আর মাটির বরফ মাঠের বরফ গাছের বরফ ছাদের বরফ ঝরনার বরফ পাহাড়ের বরফ কখনো সোনা হয়ে ওঠে রুপালি রঙের মুকুরে সোনালি মুখের ছায়ার মতো, কখনো রাঙা হয়ে ওঠে শ্বেতপদ্মিনীর কপোলে অশোকরঙা লজ্জার মতো, কখনো নীলাভ হয়ে ওঠে শ্বেতশঙ্খিনীর নয়নতারার নীল চাউনির মতো। সূর্য বিদায় নিলে চন্দ্রের পালা। চাঁদের অপলক দৃষ্টির তলে তুষারময়ী পুরী বিবশার মতো শায়িতা, তার তরুণ দেহের নিটোল কঠিন চূড়ায় চূড়ায় জ্যোৎস্নার চুম্বন, তার রজত আভরণের গাত্রে তারার ঝিকিমিকি। দন্তুর পর্বতের সারি পার্শ্বরক্ষীর মতো সারারাত্রি পাহারা দিচ্ছে, বিমুগ্ধা ‘শালে’গুলি গবাক্ষের ঘোমটা তুলে বিজলি-আলোর উঁকি মেরে দেখছে, টোপরপরা পাইন গাছের দল স্থগিতযাত্রা পদাতিকের মতো খাড়া রয়েছে।
শুধু শোভা নয়, সংগীত। এক নিশান্ত থেকে আরেক নিশান্ত অবধি মিষ্টি সুরের নহবত বাজে গ্রাম-কুক্কুটের অনবসন্ন কন্ঠে, তার সঙ্গে সুর মিলায় স্লেজবাহী অশ্বের গলার ঘণ্টা, তার সঙ্গে তাল দেয় গিরিগৃহত্যাগিনী অভিসারিণী ঝরনার ‘চল চল চল’। দিনের কাজের সঙ্গে রাতের স্বপ্নের সঙ্গে চেতনার আড়ালে ধ্বনি মিশিয়ে রয়, যারা কাজ করে স্বপ্ন দেখে তারা হয়তো শুনতে পায় না জানতে পারে না কীসে তাদের অমৃত দেয়।
কাজ? সেখানকার কাজের নাম খেলা। ডাকঘরের ছোকরা চিঠি বিলি করতে যাচ্ছে, তার গাড়িখানার না আছে চাকা না আছে ঘোড়া, দুই হাতে একবার ঠেলা দিয়ে দুই পায়ে দিলে গাড়ির মধ্যে লাফ, গাড়ি চলল বরফ-ঢাকা ঢালু রাস্তায় পিছলে, এক রাস্তার থেকে আরেক রাস্তায় বেঁকে, এক দরজার থেকে আরেক দরজায় থেমে। এক বাড়ির লোক আরেক বাড়ি যাচ্ছে, যার পিঠে চড়ে বসেছে সেটার নাম লুজ, উঁচু একখানা পিঁড়ির মতো তার আসনটা, বাঁকা দুখানা শিঙের মতো তার পায়া দুটো, চড়ে বসে পা তুলে নিয়ে হাত ছেড়ে দিলে বরফের রাস্তার ওপর ঘষতে ঘষতে চলে। যারা খেলাই করতে চায় তারা দুই পায়ে দুটো নৌকাকৃতি কাঠ বেঁধে হাতের লগি তুলে নিচ্ছে, আর দুই নৌকায় পা রেখে জমাট জলের ওপর দিয়ে রসাতলে নেমে যাচ্ছে। এরই নাম শী-খেলা (Skiing)। শুধু খেলা করতে কত দেশ থেকে কত পুরুষ কত নারী প্রতি শীতকালে সুইটজারল্যাণ্ডে আসে, বরফের ওপর দিয়ে পাহাড়ে ওঠে, শী করে, স্কেট করে, লুজে চড়ে, শ্লেজে চড়ে। কী অমিতোদ্যম স্বাস্থ্যচর্চা বলচর্চা যৌবনচর্চা! ভূতের মতন খাটতে পারে শিশুর মতন খেলতে পারে, যুবক-যুবতীর তো কথাই নেই, বৃদ্ধবৃদ্ধাদেরও উৎসাহ দেখলে মনে হয় বানপ্রস্থে গেলে এরা বনকে জ্বালাত। খাটো আর খেলো আর খাও—এই হচ্ছে এদের ত্রি-নীতি। ইউরোপে এতদিন আছি, কাঁদতে কাউকে দেখিনি, কান্নাটা এদের ধাতবিরুদ্ধ। যার মুখে সহজ হাসি নেই তার অন্তত হাসির ভান আছে, কিন্তু সহজ হাসি নেই এমন মানুষ তো দেখিনে। আরেক দিক থেকে দেখতে গেলে খুব-একটা গভীরতার দাগও কারও মুখে দেখিনে; তরঙ্গহীন শান্তি অন্তঃসলিলা অনুভূতি অতলস্পর্শী তৃপ্তি কারও চোখে-মুখে চলনে-বলনে দেহের গড়নে লক্ষ করিনে। সাত্ত্বিকতার চর্চা ইউরোপে নেই, কোনো কালে ছিল না। ইউরোপের খ্রিস্টধর্ম যিশুর ধর্ম নয়, সেন্ট পলের ধর্ম; রামের ধর্ম নয়, হনুমানের ধর্ম। তার মধ্যে বীর্য আছে, লাবণ্য নেই।
কিন্তু লাবণ্য নাই থাক, ক্লীবত্ব নেই। প্রচন্ড শীতে যে দেশে দেহের রক্ত হিম হয়ে যায়, দেহকে সে দেশে মায়া বলে কার সাধ্য? দেহরক্ষার জন্যে সে দেশে এত রকমের এত কিছু তোড়জোড় চাই যে, তার আহরণে সামান্য অনবহিত হলে ‘দেহরক্ষা’ অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্যে দেহ থেকে দেহোত্তরে উঠতে, হয় উপনিষদ লিখতে নয় মোহমুদগর লিখতে, ইউরোপের লোক কোনো দিনই পারলে না। দেহের সঙ্গে সঙ্গে মনকে নিয়ত উত্তপ্ত রাখতে যারা ব্যাপৃত, শীতল শান্তির সুযোগ-অবকাশ তাদের দেহ মনের আবহাওয়ায় কই? এদের ভিতরে বাহিরে কেবলই দ্বন্দ্ব কেবলই ব্যস্ততা, এদের মনীষীরা সত্যকে পান দ্বৈরথ সমরে, তাঁদের মনন একটা যুদ্ধক্রিয়া। এদের দেহীরা নিজেদের অভাব মেটায় প্রকৃতির স্তনে দাঁত বসিয়ে, তাদের জীবনধারণ প্রকৃতির ওপর দস্যুতায়। ইউরোপের মাটি বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য দেয় না, বিনা যত্নে তাতে নীবার ধান্য গজায় না, তার ঝরনার জল এত হিমেল যে স্টোভে গরম না-করলে ব্যবহারে লাগে না। বাল্মীকি যদি এদেশে জন্মাতেন তবে ধ্যান করতে বসে বল্মীকে নয়, বরফে ঢেকে যেতেন; বুদ্ধদেব যদি এদেশে জন্মাতেন তবে তপস্যায় বসে কোনো সুজাতার কল্যাণে ক্ষুধাশান্তি করতে পেতেন হয়তো, কিন্তু বেশিক্ষণ খালি গায়ে থাকলে তাঁকে যক্ষ্মা চিকিৎসালয়ের সুজাতাদের শুশ্রূষা গ্রহণ করতে হত।
ইউরোপের সেই নিষ্ঠুরা প্রকৃতিকে মানুষ দেবী বলে পূজা করেনি, কালী বলে তার পায়ের তলায় শব বিছিয়ে দেয়নি, তার বিষদাঁত ভেঙে তাকে নিজের বাঁশির সুরে খেলিয়েছে, তাই একদিন যে ছিল নিষ্ঠুর আজ সে-ই হয়েছে কৌতুকের। তাই বরফ পড়লে কোথায় ভয় পেয়ে ঘরে লুকিয়ে আগুন জ্বালবে, না, মানুষ বেরিয়ে পড়ল বরফের বুকের ওপর পা রেখে কালীয়দমন করতে—স্কেট করতে শী করতে লুজে চড়তে শ্লেজে চড়তে।
সুইটজারল্যাণ্ডের এই পার্বত্য পল্লিটি জেনেভা হ্রদের অনতিদূরে ও অনতিউচ্চে। প্যারিস থেকে লোজান ছাড়িয়ে মিলানের পথে ট্রিয়েস্টের অভিমুখে যে রেলপথটি এঁকেবেঁকে চলে গেছে, এগ্লের কাছে তাকে নীচে রেখে অন্য একটি রেলপথে পাহাড়ের পর পাহাড় উঠতে হয়। এই রেলপথটি শীর্ণকায় এবং এর ট্রেনগুলি ছোটো। পাহাড়ের ওপর ওঠবার সময় পেছনের দিকে ঝুঁকে পড়ে শিশুর মতো হামাগুড়ি দেয়, পোকার মতো মন্থর বেগে চলে। পথের দু-পাশে দু-সারি পাহাড় কিংবা একপাশে পাহাড় ও একপাশে খাদ। দু-পাশে পাইনের বন, বনের ফাঁক দিয়ে ঝরনা ঝরে পড়ছে। পাইনের কাঁচা চুলে পাক ধরিয়ে দিয়েছে বরফগুঁড়ো, ঝরনার পথ রোধ করে দাঁড়াচ্ছে বরফের বাঁধ।
গ্রামটি নিকট হয়ে এলে একটি দু-টি করে ‘শালে’ দেখা দেয়। ‘শালে’ (chalet) হচ্ছে এক ধরনের বাড়ি, যেমন আমাদের দেশে ‘বাংলো’। বাড়ির আগাগোড়া কাঠের, কেবল ছাদটা হয়তো শ্লেটের এবং ভিতরটা হয়তো পাথরের। প্রত্যেকটির গড়ন স্বতন্ত্র, স্থিতি ছাড়া ছাড়া, আকার বিভিন্ন এবং রঙের সমাবেশ বিচিত্র। দোচালা ছাদ, ঝুলানো বারান্দা, ছোটো গবাক্ষ, জ্যামিতিক নকশা, রঙিন আলপনা, উৎকীর্ণ উক্তি, দু-তিনশো বছর বয়স—সব মিলিয়ে প্রত্যেকটি এমন একটি বিশিষ্ট দৃশ্য যে একবার চাইলে চোখ আটকে যায়, ফিরিয়ে নেবার সাধ্য থাকে না। দেশটির প্রকৃতি এত সুন্দর, তাতেও মানুষের তৃপ্তি হল না, সে ভাবলে এমন সুন্দর আকাশ এমন সুন্দর পাহাড় এমন সুন্দর বরফ পাইন ঝরনা, দশদিকে এমন অকৃপণ সৌন্দর্য, কিন্তু এর মধ্যে আমি কোথায়? এই ভেবে সে বাইরের সৌন্দর্যের অঙ্গে অন্তরের সৌন্দর্য মাখিয়ে দিলে, সকলের অস্তিত্বের সঙ্গে নিজের অস্তিত্ব জুড়ে দিলে; বিধাতার সৃষ্টি আর মানুষের সৃষ্টি, এ বলে আমায় দ্যাখ, ও বলে আমায় দ্যাখ। তিন dimension-এর ছবির মতো বহুকোণ ‘শালে’, ধাপে ধাপে লাফ-দিয়ে-নামা পাথর বাঁধানো ঝরনা, বাঁকে বাঁকে ঘুরে-ঘুরে-নামা পাহাড়-কাটা রাস্তা, রাস্তার ধারে ধারে গাছ, রাস্তার স্থানে স্থানে বেঞ্চি, দুশো-তিনশো বছরের বাড়িতেও অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য—বিজলি আলো জলের কল সেন্ট্রাল হিটিং। ইউরোপের লোক যুগোচিত পরিবর্তন বোঝে। সেইজন্যে চার হাজার ফুট উঁচু পর্বতশ্রেণির পিঠে নিরালা একটি ছোট্ট গ্রামে বাস করে কোনো কিছুর অভাববোধ করে না। লেজাঁর পাঁচ-দশ মাইল দূরের দুটি গ্রামে বেড়িয়ে এসেছি, সেসব গ্রামেও কমবেশি এমনই স্বাচ্ছন্দ্য, অস্থায়ী পর্যটকদের জন্যে অন্তত কয়েকটি কাফে তো আছেই।
লেঁজা গ্রামটিতে দু-তিন হাজার লোকের বাস, তাদের বোধ হয় অর্ধেক নানা দিগদেশাগত যক্ষ্মারোগী। ইংরেজ আমেরিকান জার্মান ওলন্দাজ হাঙ্গেরিয়ান রুমেনিয়ান পোর্তুগিজ ইটালিয়ান জাপানি ভারতীয়—কত নাম করব। তাঁদের মধ্যে আমাদের এক বাঙালি ভদ্রলোকও আছেন, তাঁর ভাই ‘রমলা’-কার মণীন্দ্রলাল বসু মহাশয় তাঁর তত্ত্ব নেন।
যক্ষ্মা রোগের সৌরচিকিৎসার পক্ষে এই স্থানটির উপযোগিতার কারণ এখানে সূর্যের আলো প্রচুর অথচ তার আনুষঙ্গিক তাপপ্রাচুর্য নেই। শীত ও রৌদ্রের এহেন সমাবেশ অন্যত্র বিরল। পার্বত্য হাওয়া, মুক্ত প্রকৃতি, স্তব্ধ গ্রাম, পাখির গান, পাইনের মরমর, ঝরনার কলকল, বাসি শেফালির মতো অতি আলগোছে মৃদু তুষারপাত। একত্রে এত গুণ কোন শহরের ক-টা গ্রামের আছে? রোগীর জন্যে কেবল প্রাকৃতিক নয়, কৃত্রিম আনন্দেরও বহুল ব্যবস্থা হয়েছে। তাদের জন্যে ছোটো বড়ো বহুসংখ্যক ক্লিনিক; তাদের আত্মীয়দের জন্য বহুসংখ্যক হোটেল, উভয়ের জন্যে দোকান বাজার ডাকঘর ব্যাঙ্ক সিনেমা গির্জা কাফে। বড়ো ক্লিনিক ও বড়ো হোটেলগুলিতে নাচগানের বন্দোবস্ত। যারা দু-তিন বছর একাদিক্রমে শয্যাশায়ী, যাদের পাশ ফিরে শুতেও দেওয়া হয় না, তাদের নিজের নিজের ঘরে গ্রামোফোন বাজছে, কাগজপড়া হচ্ছে, খাবার পৌঁছোচ্ছে, নার্স পরিচর্যা করছে, বন্ধুরা গল্প করছে। নিজের নিজের ঘর থেকে শয্যাসমেত তুলে নিয়ে তাদের সকলকে একঠাঁই একজোট করে দেওয়া হচ্ছে, সেখানে সকলে মিলে গল্প করছে কনসার্ট শুনছে সিনেমা দেখছে এবং তাদের বন্ধু-বান্ধবীদের নাচ উপভোগ করছে।
একটি বড়ো ক্লিনিকের কথা বলি। ক্রিসমাস ট্রি স্থাপন হল, ট্রির ওপরে শতসংখ্যক মোমবাতি জ্বলে উঠল, রোগীদের শয্যাসমেত বয়ে এনে সারি করে সাজিয়ে রাখা গেল, তাদের বন্ধুবান্ধবীরা সারি বেঁধে বসলেন, কনসার্ট চলল, ধর্মোপাসনা হল, প্রসিদ্ধ ফরাসি গ্রন্থকারের স্ত্রী মাদাম দুআমেল আবৃত্তি শোনালেন। নিকোলা বুড়ো সেজে একজন এসে যতগুলি ছেলেমেয়ে সেখানে জুটেছিল তাদের সকলকে এক-একটা উপহার দিলে, সকলের সঙ্গে রঙ্গতামাশা করলে। বাতি নিভল, কনসার্ট থামল, উৎসব শেষ হল, রোগীরা নিজ নিজ ঘরে ফিরলে—অবশ্য ইতিমধ্যে সকলে কিছু পানাহার করলে।
একটি ছোটোদের ক্লিনিকের কথা বলি। ক্রিসমাস ইভে ক্রিসমাস ট্রির শাখায় শাখায় পুতুল ঝুলছে, ইলেকট্রিক আলোর নকল মোমবাতি জ্বলছে, ইংরেজ জার্মান ফরাসি ইটালিয়ান ইত্যাদি নানা জাতের নানাভাষী রুগণ ছেলেমেয়েগুলি এক-একটি শয্যায় দুজন করে শুয়েছে, তাদের আত্মীয়েরা তাদের বিছানার কাছে বসে তাদের আনন্দে যোগ দিচ্ছেন, নার্সেরা পিয়ানো বাজাচ্ছে। প্রেমিক-প্রেমিকা সেজে দুটি সুস্থ ছেলেমেয়ে গীতাভিনয় করলে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে দুটি রুগণ ছেলেমেয়েতে ডুয়েট হল, দুজন নার্স ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা সেজে রঙ্গ করলে। ছেলেরা নিকোলা বুড়োর জন্যে অধীর হয়ে উঠল। একটি নার্স এল নিকোলা বুড়ো সেজে, ‘নিকোলা এসেছে’ ‘ওই রে নিকোলা’ ‘নিকোলা…নিকোলা’ করে শোরগোল পড়ে গেল, প্রত্যেকের জন্যে নিকোলা কত উপহার বয়ে এনেছিল, বিছানায় শুয়ে শুয়ে প্রত্যেকে উপহারের ভারে চাপা পড়তে লাগল, কত রকমের খেলনা, কত রকমের ছবির বই; একজনের একটা খুদে গ্রামোফোন এনেছিল, সেটা বের করে সেএকটা খুদে রেকর্ড চড়িয়ে দিলে, সকলের তাক লেগে গেল! এতজনের এত উপহার এসেছিল যে স্বয়ং ক্লিনিকের কর্ত্রী এসে নিকোলার সাহায্য করতে লাগলেন, নার্সেরা ছুটোছুটি করে যার উপহার তার বিছানায় পৌঁছে দিতে লাগল, কারও উপহারের পর উপহারই পৌঁছোচ্ছে, কারও দেরি হচ্ছে, সে বেচারা পরের উপহার নাড়াচাড়া করে সান্ত্বনা পাচ্ছে।
বৎসরের শেষ রাত্রের উৎসব (Sylvester) সেই বড়ো ক্লিনিকে। রোগীরা সেই হলে সমবেত। প্রত্যেকেই একটা-না-একটা ফ্যান্সি পোশাক পরে এসেছে। যে রোগী দু-তিন বছর এক শয্যায় সর্বদা শুয়ে রয়েছেন তাঁরও কত শখ, তিনি রেড ইন্ডিয়ানের মতো মাথায় পালক পরেছেন, কিংবা নকল দাড়ি গোঁফ পরচুলা লাগিয়েছেন। বন্ধু-বান্ধবীরাও সেজে এসেছেন। কেউ সেজেছেন দাঁড়কাক, কেউ সেজেছেন মুসলমানি, কেউ অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি অভিজাত, কেউ রঙিন কাপড়পরা স্পেন দেশের পল্লিবাসিনী। বন্ধু-বান্ধবীদের নাচ হচ্ছে, ব্যাণ্ড বাজছে, নারীতে-পুরুষে বাহু ধরাধরি করে তালে তালে পা ফেলছে। বাজনার সুরটা এমনই যে যারা নাচছে না তাদেরও পা নেচে নেচে উঠছে। দুআমেল বললেন, নাচের বাজনার থেকে ইউরোপীয় সংগীতের বিচার করবেন না। দুআমেল আত্মস্থ প্রকৃতির স্বল্পভাষী সুপুরুষ, তাঁর Civilization গ্রন্থখানা ফ্রান্সের সুপ্রসিদ্ধ Goncourt prize পেয়েছে।
অনেকক্ষণ ধরে নাচ চলল, মাঝে মাঝে থেমে থেমে। তারপর রোগীদের খাটের কাছে বসে তাদের বন্ধু-বান্ধবীদের পানাহার ও রোগীদের শুয়ে শুয়ে যোগদান। রাত বারোটায় বছর বদলাল, দলে দলে গান গেয়ে উঠল, গ্লাসে গ্লাস ঠুকিয়ে নববর্ষের স্বাস্থ্যকামনা করলে। পানাহার শেষে আবার নাচ। ইতিমধ্যে ফ্যান্সি পোশাকের উৎকর্ষ বিচার করে যে কয়জনকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল দাঁড়কাক তাঁদের মধ্যে প্রথম।
এমনি করে ইউরোপীয়রা রোগশোককে তুচ্ছ করে, খেলার দাপটে জরাকে ভাগিয়ে দেয়। একাদিক্রমে তিন বছর এক শয্যায় শায়িত থাকা কী ভয়ানক দুর্ভোগ তা সুস্থ মানুষে কল্পনা করতে পারবেন না। এ সত্ত্বেও রোগীদের মুখে হাসি, তাদের আত্মীয়দের মুখে ভরসা, তাদের সেবিকাদের মুখে আশ্বাসনা। মৃত্যুর কাছে ব্যাধির কাছে জরার কাছে কিছুতেই হার মানব না, তালি দিয়ে গান গেয়ে হালকা তালে নেচে যাব—এই হল ইউরোপের পণ। অনাদ্যন্ত জীবনপ্রবাহে জরা ব্যাধি মৃত্যুর কতটুকুই-বা স্থান, সেই স্থানকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা কত সহস্র বৎসর ধরে বৈরাগ্য চর্চা করে আসছি। আমাদের সন্ধান সংসার হতে মুক্তি, জীবনশিখার নির্বাণ। আমাদের সাধনা দুঃখকে এড়িয়ে চলবার সাধনা, নিজেকে নিশ্চিন্ত করবার সাধনা। বুদ্ধ-শংকর-রামকৃষ্ণ কেউ তো বলেননি, ‘মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাহি।’
স্ত্রী-পুরুষের মিলিত নাচ ব্যাপারটাকে আমরা কুনীতিকর ভেবে থাকি, ইউরোপীয়রা ভাবে না। ইউরোপে প্রতিদিন নতুন নাচের আমদানি ও উদ্ভাবন চলেছে, নাচ না হলে ওদের উৎসবই হয় না। স্বাস্থ্যবান সমাজ মাত্রেই মিলিত নৃত্যের চলন আছে; আমাদের দেশের সরলপ্রকৃতি আদিমদের নাচ কত স্থানে দেখেছি, তা দেখে কুনীতির কথা মনেই ওঠেনি। অনাদিকাল থেকে যেসব সমাজে উৎসব তিথিতে স্ত্রী-পুরুষের যৌথনৃত্য প্রচলিত রয়েছে ও আশৈশব যারা একত্র নাচতে অভ্যস্ত হয়েছে, পরস্পরের অঙ্গ স্পর্শ করলে তাদের চিত্তবিক্ষেপ না-হবারই কথা। আমাদের দেশে নারী ও পুরুষ দুই স্বতন্ত্র জগতে বাস করেন, নিজের নিকট আত্মীয়-আত্মীয়া ছাড়া এত বড়ো সমাজের যত পুরুষ যত নারী সকলেই পরস্পরের কাছে অলক্ষ অস্পর্শ্য। তার ফলে নীতির দিক থেকে অস্বাস্থ্যকর কৃত্রিম কৌতূহলের সৃষ্টি ও রুচির দিক থেকে জন্মান্ধতার উদ্ভব। আমাদের রূপবোধের একদেশদর্শিতা স্পর্শবোধের অস্বাভাবিক বুভুক্ষা আমাদের সমাজকে তো ক্লীবত্বের অচলায়তন করেছেই, আমাদের সাহিত্যকেও খন্ডিত (repressed) রিরংসার ব্যবচ্ছেদাগার করে তুলছে। বিচিত্র রূপ দেখতে দেখতে, বিচিত্র গীত শুনতে শুনতে, বিচিত্র স্পর্শ পেতে পেতে মানুষের সৌন্দর্যচেতনা বাড়ে; মানুষ সৌন্দর্যবিচারক হয়; এসবের সুযোগ আমাদের সমাজে বিরল বলে আমাদের চিত্রকলা সংগীতকলা ভাস্কর্যকলা মাথা তুলতে পারলে না, আমাদের পোটোরা কেবল দু-দশটি টাইপের নারীমূর্তি আঁকেন, আমাদের অভিনেত্রীরা অবিদগ্ধা বাইজি আর ভাস্কর্য আমাদের নেই। চিত্রকরের যেমন জীবন্ত মডেল দরকার ভাস্করেরও তেমনি। আমাদের ছবিই বলো কাব্যই বলো গল্পই বলো এমন ফিকে এমন অবাস্তব এমন এক ছাঁচে ঢালা হবার কারণ কি এই নয় যে আমাদের সমাজে একটা সেক্স সম্বন্ধে আরেকটা সেক্স একান্ত স্বল্পচেতন?
বল রুমের নাচ উঁচুদরের কেন কোনো দরেরই আর্ট নয়। ওটা হচ্ছে সামাজিকতার একটা অঙ্গ, সমাজের দশজন পুরুষের সঙ্গে দশজন নারীকে পরিচিত করে দেবার একটা উপায়। যে সমাজে নিজের স্বামী বা নিজের স্ত্রী নিজেকে অর্জন করতে হয় সে সমাজে এই প্রকার পরিচয়ের সুযোগ থাকা আবশ্যক। এমন সমাজে প্রতি পুরুষের পৌরুষের ওপরে সর্বনারীর নারীত্বের দাবি যেমন প্রতি পুরুষকে বলবান প্রিয়দর্শন ও সুগঠিতদেহ হতে প্রেরণা দেয়, প্রতি নারীর নারীত্বের ওপর সর্বপুরুষের দাবি তেমনি প্রতি নারীকে রূপবতী স্বাস্থ্যবতী ও সুগঠিতদেহ হতে প্রেরণা দেয়। সর্বপুরুষের ভিতর থেকে বিশেষ করে একটি পুরুষের দাবি এবং সর্বনারীর ভিতর থেকে বিশেষ করে একটি নারীর দাবি বলবানকে করে প্রেমবান ও রূপবতীকে করে প্রেমবতী। পুরুষের সাধনা সকলকে এড়িয়ে কেবল একটি নারীর জন্যে নয়, সকলকে ছাপিয়ে বিশেষ একটি নারীর জন্যে। নারীর সাধনা সকলকে বাদ দিয়ে কেবল একটি পুরুষের জন্যে নয়, সকলকে স্বীকার করে বিশেষ একটি পুরুষের জন্যে। ইউরোপের পুরুষ একটি নৈর্ব্যক্তিক স্বামী হয়ে সুখ পায় না, সে স্বয়ংবর সভার জেতা। ইউরোপের নারীও একটি নৈর্ব্যক্তিক স্ত্রী হয়ে সুখ পায় না, সে বহুর মধ্যে বিশিষ্টা।
এ সমস্ত বাদ দিয়ে বলরুমের নাচ একটা কসরত এবং অবসর বিনোদনের একটা উপায়। ইউরোপীয় স্ত্রী-পুরুষের পা অত্যন্ত স্থূল পুষ্ট মাংসপেশিবহুল। নৃত্যকালে পরস্পরের হাত উঁচু করে ধরার ফলে বাহুরও রীতিমতো চালনা হয়। পুরুষের পক্ষে কসরতটা কিছু বেশি, কারণ সঙ্গিনীটি যদি গুরুভার হয়ে থাকেন তো সঙ্গিনীকে মোড় ফেরাবার সময় বাহুবলের অগ্নিপরীক্ষা হয়ে যায়।
বলরুম নাচের বিরুদ্ধে আমাদের দেশে নৈতিক আপত্তি শুনতে পাই। যে দেশে পরপুরুষ বা পরনারীকে চোখে দেখলে পাপ হয় ও ছোটোভাইয়ের স্ত্রীকে বড়োভাইয়ের দেখা নিষেধ, যে দেশের পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে বয়স্ক ভাইয়ের সামনে বয়স্কা বোনকে ঘোমটা দিতে হয়, সে দেশের লোক অনাত্মীয়ের সঙ্গে অনাত্মীয়ার মৌখিক আলাপেই যখন বিভীষিকা দেখে তখন দৈহিক সংঘর্ষে যে নরক দেখবে এর সন্দেহ নেই। যদি বলি ব্যাপারটা এত নির্দোষ যে ভাই-বোন বাপ-মেয়ে ও মা-ছেলে পর্যন্ত হাত ধরাধরি করে সকলের সামনে নাচে তবে হয়তো ‘উলটো বুঝলি রাম’ হবে, এদেশের পিতৃত্ব মাতৃত্ব সৌভ্রাত্রের ওপরেও সন্দেহ পড়বে। মানবচরিত্রের প্রতি যাদের সশ্রদ্ধ বিশ্বাস আছে আমাদের দেশের সেই সকল ব্যক্তিকে মনে করিয়ে দিই—মিলিত নাচ সরল প্রকৃতি আদিমদের মধ্যেও আছে এবং ইউরোপীয়রা যখন আদিম ছিল সেই সময় থেকে তাদের মধ্যে চলিত হয়ে আসছে। এটা তাদের সংস্কারগত এবং কচিবয়স থেকে বালক-বালিকা মাত্রেই এর অনুশীলন করতে শেখে। মানুষকে যাঁরা গ্রিন হাউসে পুরে সতী বা যতি বানাতে চান সেসব নীতিনিপুণদের বললে হয়তো বিশ্বাস করবেন না যে এদেশেও সতী ও যতির অপ্রতুল নেই, কিন্তু সমাজের ফরমায়েশে নয়, অন্তরের নিয়মে।
ক্লিনিকের কথায় নাচের কথা উঠল, পাঁসিঅঁর কথায় খাওয়ার কথা বলি। আমাদের পাঁসিঅঁতে (একটু ঘরোয়া ধরনের হোটলকে ফরাসিতে পাঁসিঅঁ বলে) আমরা অনেক দেশের লোক থাকতুম, যখন খাবার ঘণ্টা পড়ত তখন খাবার টেবিলে যারা সমবেত হতুম তাদের মধ্যে মণিদা ও আমি বাঙালি, অন্যদের কেউ আমেরিকান, কেউইংরেজ, কেউ জার্মান, কেউ হাঙ্গেরিয়ান, রুমেনিয়ান ফিন, ইটালিয়ান, ওলন্দাজ। এতগুলি জাতের লোক একসঙ্গে একঘণ্টা বসলেই নান দেশের কথা ওঠে। রাজনীতি অর্থনীতি আর্ট সমাজ ধর্ম সকল বিষয়ে আলোচনা চলে। আলোচনার ফাঁক দিয়ে জাতির স্বভাব ধরা পড়ে যায়, আন্তর্জাতিক জানাশোনা হয়; ফরাসিরা দেখে জার্মান মাত্রেই শয়তান নয়, আমেরিকানরা বোঝে ক্যাথরিন মেয়োর বর্ণনার সঙ্গে এই দুটি হিন্দুর মেলে না। সভাসমিতিতে সব দেশের লোক ততটা অন্তরঙ্গ ভাবে মিশতে পারে না যতটা মেশে খাবার টেবিলে। এই সত্যটা জানা থাকলে আমরা হিন্দু-মুসলমানে জনসভা না-করে জনভোজ করতুম এবং ব্রাহ্মণের ডান দিকে মুসলমানকে ও বাঁ-দিকে নমঃশূদ্রকে আসন দিয়ে দুটো মহাসমস্যার মীমাংসা দুটো দিনেই করতুম।
পরিবারের বড়ো-ছোটোতে মিলে এক টেবিলে খাবার সময় ছোটোরা বড়োদের কথা কান পেতে শোনে ও বড়োদের রীতি চোখ বুলিয়ে দেখে। আমরা যা বই পড়ে বা মাস্টারের উপদেশে শিখি এরা তা খেতে খেতেই শেখে। আমেরিকার মহিলাটির সঙ্গে জার্মানির মার্ক-মুদ্রার বিনিময় হার সম্বন্ধে কথা হচ্ছে, তাঁর বালিকা মেয়ে দুটি তা সাগ্রহে শুনছে ও সে-বিষয়ে প্রশ্ন করছে, অথচ এক্সচেঞ্জের মতো দুরূহ বিষয় যে কী, তা আমরা মা-র কাছে শেখা দূরে থাক বিএ ক্লাসের অধ্যাপক মহাশয়ের কাছে শুনেও সহজে বুঝে উঠতে পারিনে, কারণ আমাদের ঘরে ও বিষয়ে চর্চা নেই, আমাদের সমাজ বলতে কেরানি, উকিল, ডাক্তার, ইস্কুলমাস্টারের সমাজ। আমেরিকান মহিলাটি যে বেশ একজন বিদুষী তা নয়, সম্ভবত তিনিও ওসব শুনতে শুনতে শিখেছেন নিজের ঘরের ব্রেকফাস্ট টেবিলে সকলে মিলে দৈনিক পত্র পড়তে পড়তে কিংবা পরের ঘরের চায়ের টেবিলে জাহাজের ব্যাপারীদের সঙ্গে আলাপ করতে করতে। কেবল কি টাকাকড়ির কথা? ভালো-মন্দ দরকারি-অদরকারি হরেক রকমের অনেক তথ্য অনেক গুজব এবং অনেক মিথ্যাই মগজে জমিয়েছেন। জার্মান মহিলাটির স্বামী ডাক্তার, আত্মীয়েরা কেউ চিত্রকর, কেউ যোদ্ধা, কেউ ব্যবসাদার। তাঁদের সঙ্গে কথা কয়ে তাঁর নিজের শিক্ষাও ঘরে ঘরে যতটা হয়েছে স্কুলে ততটা হয়নি এবং ছবি ও গান সম্বন্ধে তিনি যেরকম রসগ্রাহিতার পরিচয় দিলেন আমাদের দেশের কোনো ডাক্তারের স্ত্রী সেরকম পারতেন না। তবে স্কুলেও যে এঁরা কেবল পড়েন না সেকথাও জানিয়ে রাখতে চাই। এঁদের প্রতি স্কুলে সংগীতশিক্ষা আদিষ্ট, প্রতি স্কুলে কলেজে প্রতি সপ্তাহে নাচের আয়োজন আছে, স্কুল থেকে এঁরা প্রত্যেকেই দুটো-একটা বিদেশি ভাষা শিখে রাখেন এবং প্রত্যেকেই কয়েকটা গৃহশিল্পের ট্রেনিং পান। ফরাসি ইংরেজি ও জার্মান এই তিনটে ভাষা ব্যবসা বা সামাজিকতার খাতিরে ইউরোপের মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রত্যেক স্ত্রী-পুরুষই অল্পবিস্তর জানেন এবং জানবার প্রধান সুযোগ পেয়েছেন নানা দেশে বেড়াবার সময় নানা দেশের লোকের সঙ্গে কাফেতে রেস্তরাঁয় হোটেলে এক টেবিলে বসে আড্ডা দিতে দিতে। এহেন আড্ডার পক্ষে সুইটজারল্যাণ্ড যেমন অনুকূল তেমন আর কোনো দেশ নয়।
ওই তো ছোট্ট একটুখানি দেশ, ওর লোকসংখ্যা ছত্রিশ লক্ষ, আয়তন আমাদের ছোটোনাগপুরের মতো হবে, তবু টুরিস্টদের দৌলতে এবং ঘড়ি ও চকোলেট বিক্রি করে ওদেশ বড়োমানুষ। ওইটুকু দেশে তিন-তিনটে ভাষা আর দু-দুটো ধর্ম চলিত, অথচ ওর ঐক্য ইতিহাসবিশ্রুত।
সুইটজারল্যাণ্ডের প্রত্যেক শহরে টুরিস্টদের জন্যে হোটেল পাঁসিঅঁ কাফে আর ব্যাঙ্ক ডাকঘর ঔষধালয় তো আছেই, প্রত্যেক স্থানে তাদের খেলার বন্দোবস্ত ও বাজারের আয়োজন আছে। সমগ্র দেশটাই যেন টুরিস্টদের জন্যে তৈরি একটা বিরাট পান্থশালা।
পৃথিবীর প্রত্যেক দেশই এখন বিজ্ঞাপন দিয়ে অন্যান্য দেশের টুরিস্টদের ডাকছে এবং দেশ দেখিয়ে তাদের পকেট হালকা করছে। ভারতবর্ষ যদি সুইটজারল্যাণ্ডের মতো উদ্যোগী হত ভারতবর্ষের দারিদ্র্য ঘুচত। কিন্তু ভারতবর্ষের এক প্রদেশের লোকই আরেক প্রদেশে সমাজ পায় না, ইউরামেরিকার টুরিস্টদের সমাজ দেবে কে? তারা যদি ইউরোপীয় হোটেলেই থাকে ইউরোপীয়দের সঙ্গেই খায় ইউরোপীয়দের সঙ্গেই খেলে ও ইউরোপীয়দের সঙ্গেই আড্ডা দেয় তবে তাদের অর্থে ভারতবাসী ধনী হবে না এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে ধারণা নিয়ে তারা দেশে ফিরবে সে ধারণা আমাদের অনুকূল হবে না। এবং দু-দশটা মুসলমান বাবুর্চি হিন্দু দোকানদার ও ফিরিঙ্গি আয়া দেখে যদি তারা ভারতবর্ষের লোক সম্বন্ধে বই লেখে তবে সে বইয়ের দেশব্যাপী প্রতিবাদ করলেই আমাদের কাজ ফুরাবে না। আমাদের সমাজের সত্যিকার পরিচয় তারা পাবে কী করে? সে যে অভিমন্যুর ব্যূহের উলটো, তার মধ্যে তাদের প্রবেশপথ কোথায়? ইউরোপের এক দেশের সমাজের সঙ্গে অন্য দেশের সমাজের মিল আছে, ভাষা জানা থাকলে এক সমাজের লোক আর এক সমাজে মিশে যেতে পারে; জাতীয় সংস্কার স্বতন্ত্র হলে কী হয়, সামাজিক আচার সর্বত্র প্রায় এক। এই বৈচিত্র্যহীনতা অনেকসময় মনকে পীড়া দেয়। আমেরিকান মহিলাটি বললেন, তিনি আমেরিকা থেকে ইউরোপে এসে নতুন কিছু দেখবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু এই যান্ত্রিকতার যুগে সমস্তই এমন এক ছাঁচে ঢালা যে ইউরামেরিকার সব দেশের পুরুষের একই পোশাক, সব দেশের নারীর একই পরিচ্ছদ—স্থলে স্থলে এমনকী একই প্যাটার্নের একই রঙের একই ভঙ্গির। কোনো লিগ অব নেশনস ফতোয়া দিয়ে এত দেশের এতগুলো মানুষকে একইরকম সাজ করতে বলেনি, কোনো মিশনারি এ বিষয়ে প্রচারকার্য করেননি, তবু কেমন করে যে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ইউরোপের রুমানিয়া অবধি প্রায় প্রতি নারীই কবরী ছেঁটে স্কার্ট ছেঁটে জামার হাত কেটে পূর্ব নারীদের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ সাজলে, সেই এক আশ্চর্য! অথচ সর্বত্র পুরুষ তার পূর্বপুরুষের মতোই জবরজং সাজে বিদ্যমান, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে রুমনিয়া অবধি তেমনি কোট ট্রাউজার্স টুপি ওভারকোট। অবশ্য ইতরবিশেষ আছে, তবু মোটামুটি বলতে গেলে সর্বত্র হোটেলমূলক সভ্যতা, গির্জামূলক ধর্ম, নাচঘরমূলক সমাজ এবং খাটা, খেলা, খাওয়া নামক ত্রিনীতি। এহেন সমাজে খাপ খেয়ে যেতে বেশি কষ্ট হয় না, এমনকী আমরা বাইরের লোকও অল্পায়াসেই এ সমাজের মধ্যে স্থান পেতে পারি।
লেঁজার পর্বতমালার নীচে জেনেভা হ্রদকে বেষ্টন করে অগণ্য পল্লি, কিন্তু তাদের প্রত্যেকটাই টুরিস্টদের জন্যে হোটেলে দোকানে ছাওয়া। এমনই এক পল্লিতে রম্যাঁ রল্যাঁ থাকেন, মণিদা ও আমি একদিন তাঁর সঙ্গে চা খেয়ে এলুম।
৫
রল্যাঁর কুটিরটির একদিকে হ্রদ অপর দিকে পর্বত। হ্রদের শাড়িটির পাড় ধরে যেমন পর্বতের পর পর্বত চলে গেছে, হ্রদের জল থেকে সোপানের মতো তেমনি পর্বতের ওপর পর্বত উঠে গেছে। হ্রদের কূলে কূলে পর্বতের মূলে মূলে পল্লির পর পল্লি। রল্যাঁদের পল্লিটির নাম Villeneuve, আর রল্যাঁর কুটিরটির নাম Villa Olga।
ভিলনভের অদূরে Chateau de Chillon নামক দ্বাদশ শতাব্দীর একটি প্রসিদ্ধ দুর্গ। বায়রনের কাব্যে এর বর্ণনা আছে, Bonnivard-কে এখানে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। দুর্গটির তিন দিকে জল, এক দিকে পর্বত। Bonnivard-এর কারাকক্ষটির গবাক্ষ থেকে যতদূর চোখ যায় কেবল জল আর আকাশ, আর উভয়ের হস্তগ্রন্থির মতো দিগবলয়। দেহকে যারা বেঁধেছিল কতটুকুই-বা তারা বেঁধেছিল! আসল মানুষটি যে চোখের ফাঁক দিয়ে সারাক্ষণই ফাঁকি দিত। বরং বন্দি ছিল তাঁর প্রহরীটা।
ভিলা অলগার একপাশে Hotel Byron নামক বৃহৎ হোটেল। রল্যাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে রবীন্দ্রনাথ নাকি এইখানে ছিলেন।
রল্যাঁর কুটিরটির বাহিরটা নিঃস্ব। দেখলে প্রত্যয় হয় না যে এত বড়ো একজন সাহিত্যিক এরকম একটা অসুন্দর ছোটো জরাজীর্ণ ‘শালে’-তে থাকেন। কিন্তু ভিতরটি সাজানো—বসবার ঘরে বই ভরা শেলফ, বই-ছড়ানো টেবিল, ফুলের সাজি, ফুল গাছের টব, দেয়ালে দেয়ালে ছবি ও দেয়াল-জোড়া পিয়ানো।
রল্যাঁর সক্ষাৎ পাবার পরমুহূর্ত পর্যন্ত মনেই জাগেনি যে তাঁর ঘরের অন্তর বাহির তাঁর নিজের অন্তর বাহিরের প্রতিরূপক!
দীর্ঘদেহ ন্যুব্জপৃষ্ঠ মানুষটি, মুখখানি লাজুকের মতো ঈষৎ নত, মুখের গড়ন উলটো-করে-ধরা পেয়ার ফলের মতো চওড়া সরু উঁচু-নীচু। প্রশস্ত উন্নত ললাট, সুদীর্ঘ শানিত নাসা, ক্ষুধিত শীর্ণ কপোল, উদগ্র সংকীর্ণ চিবুক। চোখ দুটিতে কতকালের ক্লান্তি, হরিণশিশুর নিরীহতা। ওষ্ঠে গান্ধীর চেয়েও সরল হাসি, বেদনায় পান্ডুর। সাদাসিধে পোশাক; নীলকৃষ্ণ সুট, টাই নেই, পাদরিসুলভ কলার। এক হাতে দারিদ্র্যের সঙ্গে অন্য হাতে অসত্যের সঙ্গে জীবনময় যুদ্ধ করে এসেছেন, তবু ক্ষান্তি নেই, কঠিন খাটছেন; সকাল বেলাটা শুয়ে শুয়ে লেখেন। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের জীবনী রচনায় এমন ব্যাপৃত যে, L’ame Enchantee (মন্ত্রমুগ্ধ আত্মা)-র চতুর্থ ভাগ এখনও লেখা হয়ে উঠল না।
মণীন্দ্রলাল বসুর পদ্মরাগ-এর সুখ্যাতি করলেন, Wagner-কৃত জার্মান অনুবাদ পড়েছিলেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীকান্ত-এর ভূয়সী প্রশংসা করে তাঁর সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করলেন। শ্রীকান্ত-এর ইটালিয়ান অনুবাদ হয়েছে, ফরাসি অনুবাদ হচ্ছে। দিলীপকুমার রায়ের কন্ঠে ভারতীয় সংগীত শুনে প্রীত হয়েছেন, মধ্যযুগের ইউরোপীয় ধর্মসংগীতের সঙ্গে তার সাদৃশ্য লক্ষ করেছেন, কিন্তু মধ্যযুগের পরে উভয় সংগীতের ধারা বিভিন্ন পথে প্রবাহিত হওয়ায় ভারতীয় সংগীতের সঙ্গে আধুনিক ইউরোপীয় সংগীতের বহুদূর ছাড়াছাড়ি ঘটে গেছে, এখনকার ইউরোপ ও-সংগীত গ্রহণ করবে কি না নিশ্চয় করে বলতে পারলেন না।
এতক্ষণ সহজভাবে কথা বলছিলেন আপনার লোকের মতো ঘরোয়াভাবে মৃদুমিষ্ট হেসে। যেই ভাবী যুদ্ধের সম্ভাবনার প্রসঙ্গ উঠল অমনি উত্তেজিত হয়ে পড়লেন রাজা লিয়ারের মতো। নির্বাণোম্মুখ শিখার মতো স্তিমিত নেত্রে আবেগ জ্বলে উঠল। দক্ষিণ হস্ত আবেগে উঠতে-পড়তে লাগল বেগময়ী ভাষার সঙ্গে তাল রেখে। তন্ময় হয়ে চেয়ার থেকে সরে সরে এসে খসে পড়েন বুঝিবা। গত মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ থেকে তাঁর হৃদয়ের এক স্থলে একটি ক্ষত আছে, সেই ক্ষতটিতে আঙুল ছোঁয়ালে যাতনায় অধীর হয়ে ওঠেন।
প্রতীতির সহিত বললেন, নেশনরা যতদিন-না ঠেকে শিখছে যে এক নেশনের ক্ষতিতে সব নেশনের ক্ষতি, যুদ্ধ ততদিন থাকবেই। কাতর স্বরে বললেন, মানুষের ইতিহাসে যুদ্ধের দেখছি অবসান হল না! তবু অসীম ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখলে আশার আমেজ থাকে। উদ্দীপ্ত হয়ে বললেন, আলো জ্বালান, আলো জ্বালান; দিকে দিকে আলো জ্বালিয়ে তুলুন। যুদ্ধের প্রতিষেধ শিক্ষা।
শিক্ষা সম্বন্ধে আর্টিস্টের কর্তব্য নিয়ে কথা উঠল। আর্টিস্ট কি কেবল চিরকালের সৌন্দর্য সৃষ্টি নিয়েই থাকবে না স্বকালের সমস্যা সমাধানেও সাহায্য করবে? বললেন, দুই-ই করবে। সকল যুগের জন্য কিছু, নিজের যুগের জন্যে কিছু। মানুষের মধ্যে একাধিক আত্মা আছে; কোনোটার কাজ আর্টের পূজা, কোনোটার কাজ সমাজের সেবা। যে-মানুষ আর্টিস্ট সে-মানুষ কেবল আর্ট চর্চা করে ক্ষান্ত হবে না, সে ভালোর স্বপক্ষে ও মন্দের বিপক্ষে প্রোপাগাণ্ডা করবে, ভলতেয়ার ও জোলার মতো অন্যায়ের বিরুদ্ধে মসিযুদ্ধ চালাবে। এরজন্যে যে তার যুগোত্তর সৃষ্টির ক্ষতি হবে এমন নয়, কেননা তার যুগোত্তর সৃষ্টির ভার তার যে-আত্মাটির হাতে সে-আত্মাটি কিন্তু সর্বক্ষণ সজাগ নয়।
মানুষের একাধিক আত্মা আছে একথা রল্যাঁর রচনার অনেক স্থলেই পড়েছি, তবু মানুষের অখন্ড ব্যক্তিত্বটাকে এমন খন্ড খন্ড করে দেখার প্রস্তাবে মন সায় দিলে না। তা ছাড়া সমস্যা তো প্রতি যুগেই আছে, প্রতি যুগেই থাকবে, সেজন্যে ভাববার ও খাটবার লোকও যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। আর্টিস্ট তাঁদের কাজ কেড়ে নেবে কেন? তাঁদের বাহন হবে কেন? বিশুদ্ধ আর্টের দেবী কি বড়ো সহজ দেবী? অসপত্ন পূজা না পেলে কি তিনি বরদান করেন? কালিদাসের যুগের সমস্যার জন্যে কালিদাস কী করেছিলেন? গ্যেটের যুগের সমস্যার জন্যে গ্যেটে কী করেছিলেন? জিজ্ঞাসা করলুম, শেক্সপিয়ারের যুগেও তো সমস্যা ছিল, তাঁর সৃষ্টিতে তার ছায়া দেখিনে কেন? তাঁর স্বকালের প্রতি তাঁর দায়িত্ব দেখিনে কেন? উত্তরে বললেন, কিছু কিছু দেখি বই কী। কিন্তু তাঁর যুগে হয়তো এ-যুগের মতো বড়ো কোনো সমস্যা ছিল না।
মন না মানলেও প্রতিবাদ করলুম না। এই যথেষ্ট যে, আর্টিস্টকে রল্যাঁ দেশকালের অনুরোধে বিশুদ্ধ আর্ট চর্চা মুলতুবি রাখতে বলছেন না, বিসর্জন দিতে বলছেন না, বলছেন শুধু তাই করে নিরস্ত না হতে, তাতেই আবদ্ধ না রইতে। রুশ নায়কদের মতো ফরমায়েশ দিচ্ছেন না যে, ‘হে আর্টিস্ট, তুমি যূথের মনোরঞ্জন করো, যূথতন্ত্রের জয়গান করো, বলো বন্দে যূথম’; কিংবা ভারতনায়কদের মতো ফতোয়া দিচ্ছেন না যে, ‘ঘর যখন পুড়ে যাচ্ছে তখন হে কবি, তোমার কাব্যবিলাস ছাড়ো, ফায়ার বিগ্রেডে ভরতি হও, নেহাত যদি তা না পার তো অন্যদের কর্তব্য সচেতন করতে সব রস ছেড়ে কেবল ঝাল রসের কবিতা লেখো।’ তিনি যা বলছেন তার মর্ম এই যে, মানুষের সমস্তটা যখন আর্টিস্ট নয় তখন বিশুদ্ধ আর্ট সৃষ্টির অবসরে সে অপর কিছুও করতে পারে, এবং যেহেতু তার অস্ত্র হচ্ছে লেখনী কিংবা তুলিকা সেহেতু তারই সাহায্যে সে ধর্মযুদ্ধ করলে ভালো হয়। এইটে লক্ষ করবার বিষয় যে, তিনি আর্টিস্টকে অন-আর্টিস্ট হয়ে যুগ-ঋণ শোধ করতে বললেও অন-আর্টকে আর্ট বলেননি, প্রোপাগাণ্ডাকে আর্টের থেকে পৃথক করে ষত্ব-ণত্ব জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন।
কথায় কথায় বললেন, টাকার জন্যে আর যা-ই করুন বই লিখবেন না। টাকার জন্যে অন্য খাটুনি, আনন্দের জন্যে বই-লেখা। তাঁর নিজের যৌবনে তিনি দারিদ্র্যদায়ে শিক্ষকতা করেছেন, আরও কত কী করে স্বাস্থ্য হারিয়েছেন, কষ্টার্জিত স্বল্প পরিমিত অবসর সময়কে ফাঁকি দিয়ে সরস্বতীর সেবা করেছেন, কিন্তু সরস্বতীকে ফাঁকি দিয়ে লক্ষ্মীর সেবা করেননি।
সমাজের প্রতি আর্টিস্টের দায়িত্ব প্রসঙ্গে বললেন, প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য কিছু করে কায়িক শ্রম করা। আর্টিস্টও যখন ব্যক্তি তখন আর্টিস্টেরও এই কাজ করা উচিত।
ম্যাদলিন রল্যাঁ টিপ্পনী দিলেন, স্বয়ং কায়িক শ্রম করবার অবসর পাননি বলে রল্যাঁর একটা আক্ষেপ থেকে গেছে; তাঁর শরীর ভেঙে পড়বার ওটাও একটা কারণ।
কিন্তু যে-মানুষ জগৎকে জাঁ ক্রিস্তফ দিতে পারেন সে-মানুষের শক্তি কায়িক শ্রমে অপচিত হলে কি জগৎ ক্ষতিগ্রস্ত হত না? আর্টিস্ট যদি কায়িক শ্রমে হাত দেয় তো ‘ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টে’র আশঙ্কা থাকে না কি?
ম্যাদলিন রল্যাঁ বললেন, এমন কোনো কথা নেই। এই যে তিনি অর্থাভাবে ছেলে পড়িয়ে সময় ক্ষয় করতে বাধ্য হলেন, এর বদলে যদি কায়িক শ্রম করলে চলত (অর্থাৎ অন্নবস্ত্রের জন্যে আবশ্যক অর্থ জুটত) তবে তাঁর স্বাস্থ্যের এ দশা হত না, তিনি আরও কত সৃষ্টি করতে পারতেন। তা ছাড়া তাঁর বিশ্বাস এই আত্যন্তিক স্পেশালিজেশনের যুগে সর্বমানবকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত রাখবার জন্যেও একটা কিছু দরকার, নইলে ঊর্ধ্বশ্রেণির মানুষ নিম্নশ্রেণির মানুষকে বুঝবে কী সূত্রে? যারা গতর খাটিয়ে খায় তাদের উপর থেকে যারা মাথা খাটিয়ে খায় তাদের অবজ্ঞা ঘুচবে কী করে?
বুঝলুম মহাত্মাজির সর্বভারতীয় যোগসূত্র যেমন চরকা, রল্যাঁর সর্ব-মানবিক মিলনসূত্র তেমনি কায়িক শ্রম। উভয়ের মনের এই ভাবটি টলস্টয়ের সুরে বাঁধা। শ্রমীদের ওপরে বিশ্রামীদের পরগাছাবৃত্তি পৃথিবীসুদ্ধু মানবপ্রেমিককে ভাবিয়ে তুলেছে। সমাজের যেসব দাস-মক্ষিকা এত যুগ ধরে সমাজের রানি-মক্ষিকাদের জন্যে আনন্দহীন খাটুনি খেটে এসেছে, সেই সব দলিত মানব আজ ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে। এটা হচ্ছে শূদ্র বিদ্রোহের যুগ। তারা বলছে, পেটের দায় তো প্রতি মানুষেরই আছে, একলা আমরা কেন খেটে মরব? এসো সকলে মিলে দায় ভাগ করে নিই, কায়িক শ্রম তোমরাও করো আমরাও করি। শূদ্র বিদ্রোহের এই মূল-ধুয়াটার জগৎ জুড়ে মহলা চলেছে, বৈশ্যরা ভয়ে কাঁপছেন, ক্ষত্রিয়রা ঘটা করে গোঁফে তা দিচ্ছেন, ব্রাহ্মণরা রফার উপায় খুঁজছেন।
সাময়িক একটা রফার দিক থেকে রল্যাঁ-গান্ধীর প্রস্তাবমতো প্রতি মানুষের আংশিক শূদ্রীকরণের মূল্য আছে সন্দেহ নেই। এরা না বললেও ঘটনাচক্রে বাধ্য হয়ে শূদ্রধর্ম স্বীকার করতেই হবে সকলকে! ঘটনাচক্রে বাধ্য হয়ে সকলেই একদিন ক্ষাত্রধর্ম স্বীকার করেছিল। ঘটনাচক্রে বাধ্য হয়ে সকলকেই আজ বৈশ্যধর্ম স্বীকার করতে হচ্ছে। এখনকার দিনে এমন কোনো আর্টিস্ট আছেন, ব্রাহ্মণ আছেন, যিনি অন্ন-বস্ত্রের জন্যে অর্থ উপার্জন করছেন না? কেউ আর্টের বিনিময়ে করছেন, কেউ অন্য কিছুর বিনিময়ে করছেন। আর্টের বেশ্যাবৃত্তি যাঁর কাছে নীতিবিরুদ্ধ আর্টেতরো বৈশ্যবৃত্তি তাঁর ভরসা। রল্যাঁ টাকার জন্যে বই লেখেননি, কিন্তু ইস্কুলমাস্টারি করেছেন। রবীন্দ্রনাথ টাকার জন্যে বই লেখেননি, কিন্তু জমিদারি করেছেন। দায়ে পড়ে পরধর্মের শরণ না-নিয়ে যখন উপায় নেই তখন শূদ্রোচিত কায়িক শ্রম ভালো না বৈশ্যোচিত মস্তিষ্ক-বিক্রয় ভালো? রল্যাঁর মতে প্রথমটা। যদিও কার্যত তিনি দ্বিতীয়টার আশ্রয় না-নিয়ে পারেননি। কারণ, হাতের দাসত্বের চেয়ে মাথার দাসত্বের বাজারদর বেশি—এক বলশেভিক রাশিয়া ছাড়া সর্বত্র।
কিন্তু একটা-না-একটা দাসত্ব কি করতেই হবে চিরকাল? এমন দিন কি আসবে না যেদিন মানুষ মাত্রেই সর্বতোভাবে স্রষ্টা হবে নিজের নিজের ক্ষেত্রে, বিচ্যুত হতে বাধ্য হবে না স্ব-স্ব-ধর্ম থেকে? শূদ্রত্বের অগৌরব সকলে মিলে ভাগ করে নিলে তো রোগের জড় মরে না, সকলে মিলে রোগে ভোগা যায় মাত্র। লেবারের ডিগনিটি প্রমাণ করার জন্যে সকলে মিলে ম্যানুয়াল লেবার করলে তো বেগার খাটার নিরানন্দ অপ্রমাণ হয় না, কর্মের দাসত্বকে ‘কর্তব্য’ আখ্যা দিয়ে নিজেদের ভোলানো হয় মাত্র। প্রতিভার প্রেরণায় যে মানুষ চাষ করে সুতো কাটে, সে মানুষের শূদ্রত্বে দাসত্বের গ্লানি কোথায় যে তাই ভাগ করে নেবার জন্যে রল্যাঁকে চাষ করতে হবে, রবীন্দ্রনাথকে চরকা কাটতে হবে? সমাজ ধনী হবে, যদি প্রতি মানুষের প্রতিভা পায় আপন চরিতার্থতা। বিকচ ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্য স্বীকার করে যে জটিল সামঞ্জস্যের সৃষ্টি হবে সেই সামঞ্জস্যই তো সমাজের আদর্শ, সেই তো সনাতন, সেই তো সম্পূর্ণ। চাতুর্বর্ণ্যের সাংকর্য ঘটিয়ে দিয়ে বৈচিত্র্যধ্বংসী বহিঃসাম্য স্থাপনা করলে সাময়িক একটা রফা হয় তো হয়, কিন্তু এতে মানুষের তৃপ্তি নেই। মানুষ চায় স্রষ্টৃত্বের স্বাধীনতা, এ ছাড়া আর সমস্তই তার পক্ষে দাসত্ব। শূদ্রকে দাও স্রষ্টৃত্বের স্বাধীনতা, তার শ্রম হোক তার কাছে গান গাওয়া ছবি আঁকার মতো আনন্দময়, তার শ্রমের পুরস্কারে সে রাজা হোক—কিন্তু অশূদ্রকে স্বধর্মচ্যুত করে পূর্ণত হোক অংশত হোক শূদ্র কোরো না; তার বীণা তুলি কেড়ে নিয়ে তাকে কাস্তে হাতুড়ি ধরিয়ো না; মাত্র আধ ঘণ্টার জন্যে হলেও তাকে দিয়ে চরকা কাটিয়ো না।
কায়িক শ্রম সম্বন্ধে আমার এইসব ধারণা আমি রল্যাঁকে জানাইনি। জানালে সম্ভবত তিনি বলতেন যে, একই মানুষ কি ব্রাহ্মণ শূদ্র দুই হতে পারে না? প্রতি মানুষের মধ্যে যে একাধিক আত্মা আছে। Maeterlinck নাটক লেখেন, লাঙল ঠেলেন, মৌমাছি ও পিঁপড়েদের তদারক করে প্রামাণ্য বিজ্ঞানগ্রন্থ লেখেন—তাঁর তা হলে গোটা তিনেক আত্মা। কোনোরকম কায়িক শ্রমের প্রতি যার একটাও আত্মার একটুও রুচি নেই এমন মানুষ সম্ভবত একজনও পাওয়া যাবে না।
এমন যদি তিনি বলতেন তবে আমি আপত্তি করতুম না। নিজেকে নানাদিকে কুশলী করবার সাধ মানুষ মাত্রেই আছে। এই সাধ যদি মানুষ মাত্রকেই সুতোকাটা নামক কাজটিতে কৃতী হতে প্রেরণা দেয় তবেই সে চরকা ধরবে নতুবা স্পেশালিজেশনের প্রতিকার স্বরূপ কিংবা সর্বতোভাবে আত্মসম্পূর্ণ হবার দুরাশায় কিংবা সর্বমানবের সঙ্গে যুক্ত হবার ধারণায় যদি ধরে বা ধরতে বাধ্য হয় তবে সেটা হবে তার সৃষ্টির সতিন, তার অন্তরের দাসত্ব। আধ ঘণ্টার জন্যে হলেও সেটা তার স্বাধীনতার শ্বাসরোধী। সার্বজনীন দাসত্বের দ্বারা সর্বমানবের যে একীকরণ সে-মন্ত্রের উদগাতা যদি রল্যাঁ-গান্ধী-টলস্টয়ও হন তবু সেটা ছদ্মবেশী জড়বাদ।
মণীন্দ্রলাল জিজ্ঞাসা করলেন, এ যুগের লোক কাব্য পড়ে না কেন? রল্যাঁ বললেন, এ যুগের লোকের দুঃখ-সুখের কথা কেউ কাব্যে লেখে না বলে। ভিক্টর উগোর মতো জনসাধারণের কবি থাকলে জনসাধারণ কাব্য পড়ত বই কী।
এবার তাঁর মনের আরেকটা কোণ ছোঁয়া গেল। তাঁর কাছে আর্টের অভীষ্ট সমঝদার, আলটিমেট সমঝদার—জনসাধারণ। জনসাধারণের জন্যেই আর্ট। তিনিই একদিন People’s Theatre-এর পরিকল্পনা দিয়েছিলেন। যা-কিছু সুন্দর যা-কিছু শিব তা থেকে যদি একজন মানুষও বঞ্চিত থাকে তবে আর্টিস্টের আনন্দ অপূর্ণ থেকে যায়। তা বলে তিনি কোথাও এমন বলেননি যে, জনসাধারণের আর্ট জনসাধারণের দিকে নেমে যাবে। অন্যত্র তিনি বলেছেন, খাঁটি আর্টের আবেদন এমন গভীর যে, নিম্নতম অধিকারীর হৃদয়ও তাতে সাড়া দেয়। প্রমাণ, শেক্সপিয়রের নাটক। ও-জিনিস বোঝবার জন্যে বৈদগ্ধ্যের দরকার থাকতে পারে, কিন্তু বোধ করবার পক্ষে প্রকৃতি যা দিয়েছে তাই যথেষ্ট। শেক্সপিয়র দেখবার জন্যে ইতর সাধারণের আগ্রহ শিক্ষিতদের আগ্রহকে ছাড়িয়ে যায়।
চা খেতে খেতে শেষ কথা হল সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে। সাহিত্যের প্রভাবে যদি নৈতিক অরাজকতা ঘটে তবে তারজন্যে কি সাহিত্যিক দায়ী হবে? বললেন, ধর্মের প্রভাবে জগতে কত যুদ্ধই ঘটে গেছে তারজন্যে কি কেউ ধর্মসংস্থাপকদের দায়ী করে? সাহিত্যিক যদি সুস্থমনা হয়ে থাকে তবে সমাজের সত্যিকার আদর্শের সঙ্গে সাহিত্যের সত্যিকার আদর্শের বিরোধ হবে না; আর যদি অসুস্থমনা হয়ে থাকে তবে তার রচনাকে সাহিত্য নাম দিয়ে সাহিত্যকে সাজা দেওয়া সাজে না।
রল্যাঁর কথাগুলির প্রতিলিপি দিতে পারলুম না, ভাবছায়া দিলুম। এইখানে বলে রাখি যে, এই আলাপ-আলোচনার অধিকাংশই হয়েছিল মণি দা-তে ও রল্যাঁ-তে; এবং আমি ফরাসি ভালো না-বুঝতে পারায় তথা রল্যাঁ ইংরেজি আদৌ না-বলতে পারায় মণি-দার ও কুমারী রল্যাঁর ওপরে আমাকে এতটা নির্ভর করতে হয়েছে যে, এই লেখায় অনেক ভুলচুক থেকে গিয়ে থাকতে পারে। তবু মোটের ওপর এতে কিছু এসে যাবে না এইজন্যে যে, এই আলাপ-আলোচনার আগে ও পরে বহু বার আমি রল্যাঁর মতবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিত হয়েছি। এসব তাঁর মুখে নতুন শুনলুম এমন নয়। আমরা তাঁর কথা শুনতে যাইনি, আমরা গিয়েছিলুম তাঁকে শুনতে ও তাঁকে দেখতে। কাব্য পড়ে যেমন ভাবি কবি তেমন কি না, এইটি জানবার জন্যে প্রত্যেকেরই একটি স্বাভাবিক কৌতূহল থাকে। সৃষ্টি দেখে স্রষ্টার যে-কল্পমূর্তিটি গড়া যায় বাস্তবের সঙ্গে তার তুলনা করে না-দেখা পর্যন্ত যেন সৃষ্টিটাকেই পূর্ণরূপে দেখা হয় না।
জাঁ ক্রিস্তফের স্রষ্টাকে তাঁর ফোটোর সঙ্গে মিলিয়ে মনে মনে যে কল্পমূর্তিটিকে গড়েছিলুম সে-মূর্তিটিকে ভেঙে ফেলতে হল বলে দুঃখ হল, কিন্তু মানুষটিকে ভালোবাসতে বাধল না। বলিষ্ঠমনা পুরুষের বাহিরটা বলিষ্ঠদেহ পুরুষের মতো হয়ে থাকলে শ্রদ্ধা বাড়ত, কিন্তু ঐশ্বর্যময় মনের বাহিরটা শিশু ভোলানাথের মতো দেখে মমতা জন্মাল। দেহে-মনে সুসমঞ্জস পার্সোন্যালিটি বলতে একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি; গান্ধীকে দেখে নিরাশ হয়েছিলুম, রল্যাঁকে দেখে হলুম। এঁদের দেহ এঁদের মনের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে ও আগুনকে ঢেকেছে; সন্ন্যাসীর গায়ের বিভূতি যেমন তার অন্তরের তপস্যাকে ঢাকে। কিন্তু যেমন গান্ধীর প্রতি তেমনি রল্যাঁর প্রতি এমন একটি মমতা জাগল যেমনটি নিছক গুণীব্যক্তির প্রতি জাগে না। ভালোবাসা ও ভালোলাগার মধ্যে কোনখানে যে একটি সূক্ষ্ম রেখা আছে চিন্তা করে তার নিরিখ পাইনে, বোধ করে তার অস্তিত্ব জানি। এক-একটা বিরাট পার্সোন্যালিটির সংস্পর্শে এলে এই বোধ-ক্রিয়াটি একান্ত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।
৬
ফরাসিদের পারি নগরীর নামে পৃথিবীসুদ্ধ লোক মায়াপুরীর স্বপ্ন দেখে। আরব্য রজনির বাগদাদ আর কথাসাহিত্যের পারি উভয়েরই সম্বন্ধে বলা চলে, ‘অর্ধেক নগরী তুমি অর্ধেক কল্পনা।’ পৃথিবীর ইতিহাসে পারির তুলনা নেই। দুই হাজার বৎসর তার বয়স, তবু চুল তার পাকল না। কত বার তাকে কেন্দ্র করে কত দিগবিজয়ীর সাম্রাজ্য বিস্তৃত হল, কত বার তার পথে পথে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার রক্তগঙ্গা ছুটল, কত ত্যাগী ও কত ভোগী, কত জ্ঞানী ও কত কর্মী, কত রসজ্ঞ ও কত দুঃসাহসী, বিপ্লবে ও সৃষ্টিতে স্বাধীনতায় ও প্রেমে তাকে অমর মানবের অমরাবতী করলেন, সাহিত্যে চিত্রকলায় ভাস্কর্যে নাট্যকলায় সুগন্ধি শিল্পে পরিচ্ছদকলায় স্থাপত্য ও বাস্তুকলায় সে সভ্যজগতের শীর্ষে উঠল। পারিই তো আধুনিক সভ্যতার সত্যিকারের রাজধানী, অগ্রসরদের তপস্যাস্থল, অনুসারকদের তীর্থ। এর একটি দ্বার প্রতি দেশের কাঞ্চনবান সম্ভোগপ্রার্থীদের জন্যে খোলা, অন্য দ্বারটি প্রতি দেশের নিঃসম্বল শিল্পী ভাবুক বিদ্যার্থীদের জন্যে মুক্ত। একদিক থেকে দেখতে গেলে পারি রূপোপজীবিনী, আমেরিকান টুরিস্টদের হিরে-জহরতে এর সর্বাঙ্গ বাঁধা পড়েছে, তবু জাপান অস্ট্রেলিয়া আর্জেন্টিনা থেকেও শৌখিন বাবুরা আসেন এর দ্বার-গোড়ায় ধরনা দিয়ে একটা চাউনি বা একটু হাসির উচ্ছিষ্ট কুড়োতে। অন্যদিক থেকে দেখতে গেলে পারি অন্নপূর্ণা, সর্বদেশের পলাতকদের আশ্রয়দাত্রী, তার জাতিবিদ্বেষ নেই, সে পোল রুশ রুমানিয়ানকেও শ্রমের বিনিময়ে অন্ন দেয়, নিগ্রোকেও শ্বেত-সেনার নায়ক করে এবং নানা দেশের যে অসংখ্য বিদ্যার্থীতে তার প্রাঙ্গণ ভরে গেছে তাদের কত বিদ্যার্থীকে সে বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে জীবিকাও জোগায়।
পৃথিবীর অন্য কোনো নগর দেখতে পৃথিবীর এত দেশের এত টুরিস্ট আসে না; পারি দেখতে প্রতি বৎসর যে কয় লক্ষ বিদেশি আসে, তাদের পনেরো আনা আমেরিকান ও ইংরেজ। আমেরিকানদের চোখে পারিই হচ্ছে ইউরোপের রাজধানী, আর ইউরোপের লোকের চোখে পারি হচ্ছে লণ্ডন ভিয়েনা বার্লিন মস্কোর চেয়েও আন্তর্জাতিক। আমেরিকান বিদ্যার্থীতে পারি ছেয়ে গেছে, আর ইউরোপের নানা দেশের বিদ্যার্থীদের কাছে পারি চিরকালই আমাদের কাশীর মতো কালচার-পীঠ। শুধু কাশী নয় কামরূপও বটে, যত রাজ্যের রোমান্সপিপাসু এই নগরীতেই তীর্থ করতে আসে।
আয়তনে ও লোকসংখ্যায় পারি লণ্ডনের প্রায় অর্ধেক, কলকাতার প্রায় তিনগুণ। আজকালকার দিনে একটা শহরের সঙ্গে আরেকটা শহরের বাইরে থেকে যে তফাত সেটা ছোটোভাইয়ের সঙ্গে বড়োভাইয়ের তফাত, বয়স ও বৃদ্ধির উনিশ-বিশ থাকলেও পারিবারিক সাদৃশ্য উভয়েরই মুখে।
পারিতে ট্রাম মেট্রো বাস ট্যাক্সি ধোঁয়া কাদা বস্তি ব্যারাক লণ্ডনের মতো সমস্তই আছে, কিন্তু মোটর গাড়ি কিছু বেশিসংখ্যক, বাড়িগুলো কিছু স্বাধীন গড়নের, কাদাটা কিছু গভীর ও গাঢ়। মোটের ওপর পারি লণ্ডনের মতো ফিটফাট নয়, বেশ একটু নোংরা এবং অনেক বেশি গরিব। উঁচু দরের বাস্তুকলা তার কয়েকটি প্রাসাদে সৌধে থাকলেও লণ্ডনের সৌষ্ঠব তার অধিকাংশ বাড়ির নেই। ঐতিহাসিক প্রাসাদ সৌধের ছবি দেখে পারিকে যা ভাবি সর্বসাধারণের বাসগৃহ দেখলে সে কল্পনা ছুটে যায়। কিন্তু পারির আসল সৌন্দর্য তার প্রশস্ত সরল রাজপথগুলি, তার বৃহৎ চতুষ্কোণ প্লাসগুলি, তার সপ্তসেতুবেষ্টিত সর্পিণী নদীটি, সর্পিণীর দুই রসনার মতো সেন নদীর দুটি অর্ধের মধ্যবর্তী দ্বীপটি এবং নগরীর দুই উপান্তের প্রমোদোদ্যান দুটি।
পারিতে লণ্ডনের মতো পার্ক বিরল; তবে তার এক-একটি রাজপথ এক-একটি সরলরেখাকৃতি পার্ক বিশেষ। পারির নিতান্ত মাঝারি রাজপথগুলিও সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর চেয়ে চওড়া। ‘সাঁজেলিসি’-র এক পাশ থেকে আর এক পাশ দেখা যায় না, পাশাপাশি দশটা চৌরঙ্গির মতো। সে তো একটি রাজপথ নয়, একসঙ্গে অনেকগুলি রাজপথ; রাজপথের মাঝখানে এক সারি বাগান, রাজপথের ওপরে এক-একটি দোকান বা প্রাসাদ বা থিয়েটার। এক-একটা বুলভার্দ এক-একটা বিরাট ব্যাপার, যেমন দীর্ঘ তেমনি প্রস্থ। অধিকাংশ রাস্তার সম্বন্ধে একথা খাটে যে, একটি রাস্তা মানে একটি রাস্তা নয়, সমান্তরাল দুটি-তিনটি রাস্তা, কোনো কোনো স্থলে পাঁচটি রাস্তা। অর্থাৎ প্রতি রাস্তার অনেকগুলি করে ভাগ আছে, যেমন ইন্দ্রধনুর সাতটি ভাগ। প্রথমে ফুটপাথ, ফুটপাথের পরে রাস্তা, রাস্তার পরে গাছের সারি, গাছের সারির পরে ঘোড়দৌড়ের রাস্তা, সে রাস্তার পরে গাছের সারি ও বসবার বেঞ্চি, তারপরে আবার ঘোড়দৌড়ের রাস্তা, তারপরে আবার গাছের পার্টিশন, তারপরে আবার রাস্তা, তারপরে আবার ফুটপাথ। সব রাস্তার অবশ্য একইরকম ভাগ নয়, তবে অধিকাংশ রাস্তাই অসাধারণ চওড়া আর অনেক রাস্তার ফুটপাথের ওপরে স্থলে স্থলে ছোটো ছোটো দোকান আছে, যেমন পুরীর ‘বড়ো দান্তের’-র ওপরে অস্থায়ী ছোটো ছোটো দোকান। এক-একটা ফুটপাথও রাস্তার মতো চওড়া, স্থলে স্থলে এইসব দ্বীপের মতো দোকান, অধিকাংশ ছেলেদের খেলনার বা মেয়েদের এটা-ওটার দোকান। ঠিক আমাদের দেশের মতো সেসব দোকান; ভিড় জমেছে, দরদস্তুর চলেছে, হইচই হট্টগোল।
আমাদের সঙ্গে ফরাসি, ইটালিয়ান প্রভৃতি দক্ষিণ ইউরোপীয়দের প্রকৃতিগত মিল আছে। এরাও খুব গোলমাল ভালোবাসে, অতিরিক্ত রকম বাচাল, আর বাদশাহি রকমের কুঁড়ে। কুঁড়ে বললে বোধ হয় ভুল বলা হয়, বরং বলি বিশ্রামপ্রিয়। সময়ের দাম এরা ইংরেজ আমেরিকানদের মতো বোঝে না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিয়ে কাটিয়ে দেয়। তা বলে এরা বড়ো কম খাটে না। পারির যারা আসল অধিবাসী, খুব খাটতে পারে বলে তাদের সুনাম আছে। মেয়েরা গল্প করবার সময়েও জামা সেলাই করছে—শৌখিন জামা। জামাকাপড়ের সখটা ফরাসিদের অসম্ভব রকম বেশি, বিশেষ করে ফরাসি মেয়েদের ও শিশুদের। পুরুষরা কতকটা বেপরোয়া। তাদের প্রধান সম্পদ তাদের জাঁদরেলি গোঁফ, তাদের সেই ব্রহ্মাস্ত্রটিতে শান দেবার দিকে তাদের যত নজর তত নজর তাদের স্নান না-করা গাত্রের দিকে নেই। সুগন্ধিশিল্প পারিকে আশ্রয় করবার কারণ হয়তো এই। হ্যাঁ, পারির লোক খুব খাটতে পারে বটে। খুব ভোরে উঠে খাটতে আরম্ভ করে দেয়, অনেক রাত অবধি খাটে, কিন্তু পানাহারটা সেই অনুপাতে ঘটা করেই করে। এরা ব্রেকফাস্ট বেশি খায় না, লাঞ্চটা ইংল্যাণ্ডের তুলনায় বেশি খায়, আর ডিনারটা ইংল্যাণ্ডের তুলনায় রাত করে খায়। আহার সম্বন্ধে এদের মোগলাই রুচি, গোপালের মতো যাহা পায় তাহা খায় না। রন্ধনশিল্প ইউরোপের কোথাও থাকে তো পারিতে। এত রকমের খাদ্য এত সস্তায় কেন অনেক দাম দিয়েও লণ্ডনে পাবার জো নেই। দুনিয়ার সব দেশের খানার এরা সমঝদার, সেইজন্যে যেকোনো রেস্তরাঁয় সব নেশনের খাদ্যের একটা-না-একটা নমুনা পাওয়া যাবেই। সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, পারিতে অত্যল্প খরচে অনেকখানি তৃপ্তির সহিত খেতে পারা যায়। রান্নাটা উঁচু দরের তো বটেই, রান্নাটা টাটকা। শাকসবজি ও মাংসের জন্যে ইংল্যাণ্ড অন্য দেশের মুখাপেক্ষী, ফ্রান্স তেমন নয়।
এ তো গেল আহার তত্ত্ব। ফরাসিরা পাননিপুণও বটে। যেকোনো রেস্তরাঁয় গেলে ভোজ্য তালিকার সঙ্গে সঙ্গে একটা পানীয় তালিকাও দেয়। ও-রসে বঞ্চিত বলে খাঁটি খবর দিতে পারব না, কিন্তু সেজন্যে অপদস্থ হয়েছি পদে পদে। এ কেমন মানুষ যে ‘ভ্যাঁ’ খায় না? এই ভেবে ওরা হাঁ করে তাকায়। আমি মনে করেছিলুম ইংরেজরাই ভারি মদ খায়, কেননা লণ্ডনের অলিতে-গলিতে ‘পাবলিক বার’। ও হরি! পারির গলিতে গলিতে যে একটা নয় দুটো নয় পঞ্চাশটা কাফে! লণ্ডনে কাফে নেই, কাফে নামধেয় যা আছে আসলে তা রেস্তরাঁ, লণ্ডনের রেস্তরাঁ; সংখ্যা পারির তুলনায় আঙুলে গোনা যায়।
এই কাফে জিনিসটি ফরাসি সভ্যতার একটা অঙ্গ। ফ্রান্সের আধুনিক ইতিহাস তার কাফেগুলিতেই তৈরি হয়েছে, ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস যেমন তৈরি হয়েছে তার ইস্কুলগুলির প্লেগ্রাউণ্ডগুলিতে! পঞ্চাঙ্ক নাটকের মতো যতগুলি বিপ্লবের অভিনয় পারিতে হয়ে গেছে সকলগুলির রিহার্সাল হয়েছিল কাফেগুলিতে; কাফেই হচ্ছে ফরাসিদের চন্ডীমন্ডপ, ফরাসিদের ক্লাব। কাফেতে গিয়ে এক পেয়ালা কাফি বা শোকোলা (‘Chocolat’) বা হালকা মদের ফরমাশ করে যতক্ষণ খুশি বসে আড্ডা দাও—দু-ঘণ্টা তিন ঘণ্টা পাঁচ ঘণ্টা! তাস খেলো, দাবা খেলো, গানবাজনা শোনো, কাগজ পড়ো, চিঠি লেখো; ছাত্র হয়ে থাকো তো পড়া করো। কাফেতে একবার গিয়ে বসলে আর উঠতে ইচ্ছে করে না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলতে থাকে ইয়ার্কি দেওয়া, ফ্লার্ট করা। একটু-আধটু নেশায় ধরলে রঙ্গকৌতুক থেকে মাথা ফাটাফাটি পর্যন্ত উদারা মুদারা তারা। ওরই মধ্যে একটু স্থান করে নিয়ে একটু-আধটু নাচাও স্থল বিশেষে হয়। অনেক তপস্বীর তপস্যা আর অনেক কুঁড়ের কুঁড়েমি দুই-ই একসঙ্গে চলতে থাকে যখন, তখন একথা বিশ্বাস হয় না যে এদের কেউ কোনোদিন জগৎকে ধন্য করে দেবে চিন্তাবৈশিষ্ট্যে, অবাক করে দেবে কর্মনেতৃত্বে, মুগ্ধ করে দেবে অভিনেত্রীরূপে। তখন এই কথা মনে হয় যে, এদের যেমন খাটুনির সীমা নেই তেমনি কুঁড়েমিরও সীমা সেই—ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেবল মজলিশি রসিকতা আর মজলিশি আদবকায়দা আর মজলিশি সুরাপান।
এই একটা মস্ত জিনিস যে কাফে ভয়ানক সস্তা, দু-চার আনা খরচ করে দু-ঘণ্টা এক স্থানে বসা ও প্রাণ খুলে গল্প করা; লণ্ডনে এমন সুযোগ নেই। আমাদের দেশে চায়ের দোকানগুলোতে তর্কসভা বসে, সেইগুলোই আমাদের ভাবী যুগের কাফে। তাই থেকে আমাদের ভাবী সাহিত্যিকদের উদ্ভব হবে, ভাবী রাষ্ট্রনেতাদের অভ্যুত্থান ঘটবে। ব্যয়সাধ্য ক্লাব যে আমাদের মাটিতে শিকড় গেড়ে আমাদের বট-অশ্বত্থের মতো দীর্ঘজীবী হবে এমন আমার মনে হয় না। ওই চায়ের আড্ডাগুলোর সঙ্গে একটা করে পাঠাগার জুড়ে দিলে ওইগুলোই হবে জনসাধারণের বিশ্রাম, আমোদ ও শিক্ষার স্থান।
কাফের মতো ‘পাতিসেরি’গুলোতেও আড্ডা বসে। পাতিসেরি মানে কেক রুটির দোকান, ওখানে গিয়ে কেক কিনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতে পারা যায়। অনেক পাতিসেরিতে চা-কফি খাবার জন্যে একটু ঠাঁই করে দেওয়া হয়, সেই সুযোগে গল্প জমে, তর্ক ওঠে, আলাপ পরিচয় হয়, দেশের মানুষ দেশের মানুষকে চিনতে চিনতে দেশকে চেনে, বিদেশের মানুষকে চিনতে চিনতে বিদেশকে চেনে। ফরাসিরা ইংরেজদের মতো নীরবপ্রকৃতি নয়, গম্ভীরপ্রকৃতি নয়; ওরা ভদ্রতার খাতিরে আবহাওয়া সম্বন্ধে দু-একটা তুচ্ছ প্রশ্ন করে চুপ করে না, ওরা বকে আর বকায়।
পারির লোক জন্ম-রসিক। আমোদের জন্যে এমন অকৃপণ ব্যবস্থা কুত্রাপি নেই। অবশ্য আমোদ মাত্রেই বিশুদ্ধ নিষ্পাপ হরিনাম জপ করা নয়, বরং বহুক্ষেত্রে পঙ্কিল। পথে ঘাটে জুয়োর আড্ডা। এ আপদ লণ্ডনে নেই। পথে ঘাটে নাগরদোলা প্রভৃতি শিশুসুলভ কৌতুক। খেলাধুলার রেওয়াজ ইংল্যাণ্ডের মতো নেই। ইংল্যাণ্ডে মাঠে মাঠে ফুটবল খেলা, টেনিস খেলা, সাঁতার। ইংরেজরা জন্ম খেলোয়াড়। স্বাস্থ্যচর্চাটাকেই ওরা চরম বলে জেনেছে। ওইখানে ওদের জিত।
পারিতে অন্তত বিশটি উঁচু দরের থিয়েটার আছে। এ ছাড়া সিনেমা, ‘কাবারে’ (cabaret), সংগীতশালাও আছে অগুনতি। ‘কাবারে’গুলি পারির বিশেষত্ব, লণ্ডনে নেই, লণ্ডনে প্রবর্তন করবার প্রস্তাব অনেকে করছেন। এর সঙ্গেও ফরাসি ইতিহাসের যোগ আছে, কেননা এতে যেসব নাচ তামাশা হয়, সেসব অনেকসময় পলিটিক্যাল ব্যঙ্গবিদ্রূপ। সংগীতশালা পর্যায়ভুক্ত এমন সব রঙ্গালয় আছে যেখানে কেবল দৃশ্যের পর দৃশ্য দেখানো হয়, কোনোটার সঙ্গে কোনোটার সম্বন্ধ নেই, এবং দৃশ্যের সঙ্গে বাদ্য আছে কিন্তু কথা নেই। একে বলে ‘revue’, এ জিনিস লণ্ডনেও প্রবর্তিত হয়েছে, কিন্তু এ জিনিস আসরে নামাতে অনেক টাকা অনেক বুদ্ধি ও অনেকখানি ‘নির্লজ্জতা’ দরকার। এ সকলের সমন্বয় লণ্ডনে দুর্লভ, লণ্ডনের লোক এক নম্বরের শুচিবায়ুগ্রস্ত। পারির লোক বিবসনা স্ত্রীমূর্তি দেখে শকড হবে এমন কচি খোকা নয়। তারা অতি অল্প বয়স থেকে পারির দশ-বারোটা মিউজিয়ামে গ্রিক ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দেখে চোখকে শিক্ষিত ও চিত্তকে নির্বিক্ষেপ করেছে। তারা রুশো ভলতেয়ার ও জোলা-ফ্লোবেয়ারের রচনা পড়ে সুনীতি-দুর্নীতি ও সুরুচি-কুরুচির হিসাব-নিকাশ করে রেখেছে। তারা আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যের নাগরিক, ন্যাকামি বা নাসিকা-সিটকারকে তারা উচ্চাঙ্গের মর্যালিটি বলে না; তারা সুন্দরের সমঝদার, মানবদেহকেও সুন্দর বলে জানে। ‘মুল্যাঁ রুজ’ বা ‘ফোলি বেরজেয়ারে’ অর্ধ-বিবসনাদের নির্নিমেষনেত্রে নিরীক্ষণ করে শকড হতে পিউরিটান নিউ ইংল্যাণ্ডের টুরিস্টরা দলে দলে যান, আসল ফরাসিরা যায় কি না সন্দেহ; যদি-বা যায় নৃত্যনৈপুণ্য খুঁটিয়ে বিচার করবার মতো শিক্ষা নিয়ে যায়, কেবল এক জোড়া কৌতূহলী চক্ষু ও একটা শুচিবায়ুগ্রস্ত মন নিয়ে যায় না। পারির বহুসংখ্যক প্রমোদাগার বিদেশিদের জন্যেই অভিপ্রেত এবং তাদেরই দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত। মার্কিনের টাকার লোভে মার্কিনের বৈশ্যসুলভ স্থূল রুচির ফরমাশ তারা খাটছে। এই আভিজাত্যহীন পঙ্করসবোধ, এই চর্চা অবসরহীন পল্লবগ্রাহী সমঝদারি, এই অবিশ্রান্ত অফুরন্ত থ্রিল-পিপাসা ফরাসি কালচারকে ডলারের গোলা মেরে উড়িয়ে দিতে বসেছে, এর আক্রমণে ফরাসিদের বিশুদ্ধ আর্ট হয়তো আর বেশিদিন টিকবে না, ফরাসি সভ্যতার সরস্বতী অবশেষে বাইজির মতো সস্তা গান শুনিয়ে ও সস্তা নাচ নেচে সরাব পান করে নাসিকাধ্বনি করবেন। ফরাসি জাতিটার অমেয় জীবনীশক্তির ওপরে আমার অটল আস্থা আছে বলেই যা আশা চতুর্দশ লুই ও প্রথম নাপোলেঅঁর দেশ এই নতুন আঘাতকেও যথাকালে কাটিয়ে উঠবে, এই বিষয়কেও পরিপাক করবে নীলকন্ঠেরমতো।
ফরাসিরা একটা আত্মবিপরীত জাতি, তাদের ধাতটা এক্সট্রিমিস্ট, তারা দু-দল চরমপন্থীর সমন্বয়—গোঁড়া ক্যাথলিক আর গোঁড়া যুক্তিবাদী। যারা মানে তারা সমস্ত মানে, ঈশ্বর, শয়তান, স্বর্গ, নরক, যিশু, যিশুর কুমারী মাতা, পোপ কনফেসন, প্রতিমা, কর্মকান্ড। যারা মানে না তারা কিছুই মানে না, তারা জ্ঞানমার্গের নাইহিলিস্ট, তারা বদ্ধ সিনিক, তারা পাঁড় এপিকিয়োর। জাতটা অতিমাত্রায় শক্তের ভক্ত অথচ নৈরাজ্যবাদী। বাঙালি জাতটার সঙ্গে এ বিষয়ে এদের মিল আছে—যেমন ইমোশনাল তেমনি নাস্তিক, যারা মানে তারা মন দিয়ে মানে না, হৃদয় দিয়ে মানে; যারা মানে না তারা মন দিয়ে উড়িয়ে দেয়, হৃদয় দিয়ে পারে না। নইলে আনাতোল ফ্রাঁসের মতো তীক্ষ্ণদৃষ্টি পুরুষ কখনো গত মহাযুদ্ধের মতো নির্বোধ একটা ব্যাপারের তলা পর্যন্ত দেখেও সস্তা পেট্রিয়টিজমের ঢাক পিটোতে যান।
গোঁড়া ধার্মিক হোক, গোঁড়া অধার্মিক হোক, রসবোধ জিনিসটা এদের জাতিগত; ও জিনিস এরা খ্রিস্টধর্মের মতো বাইরে থেকে পায়নি বলে ও নিয়ে এরা ঝগড়া করে না। Venus de Milo-র উলঙ্গ সৌন্দর্য এরা পিতা-পুত্র মিলে দেখে এবং পিতা-পুত্রে মিলে আলোচনা করে। উলঙ্গতা নিয়ে তর্ক বাঁধে না, ওটা চোখসওয়া হয়ে গেছে, ওটা উভয় পক্ষেই আবশ্যক বলে ধরে নিয়েছে; তর্ক বাঁধে সৌন্দর্য নিয়ে। এই প্রসঙ্গে বললে অবান্তর হবে না যে, দক্ষিণ ইউরোপের সঙ্গে উত্তর ইউরোপের এইখানে একটা তফাত আছে। ফরাসি, ইটালীয়, গ্রিক প্রভৃতি জাতিরা দেহকে প্রগাঢ় ভালোবাসে ও ভক্তি করে, সহজিয়াদের মতো দেহের মধ্যে তত্ত্ব খুঁজে পায়। এরা প্রতিমাপূজক জাতি, এদের দেবতারা সশরীরী, এদের শিল্পীরা যখন মাতৃমূর্তি আঁকে তখন স্তনের ওপরে বস্ত্র টেনে দেয় না, যখন বালক যিশু আঁকে তখন খামোখা কৌপীন পরিয়ে দেয় না, বাস্তবকে স্বীকার করে নিয়ে তার ওপরে এরা সৃষ্টি খাড়া করে, মাতৃমূর্তির মুখে তৃপ্তি ফুটিয়ে তোলে। উত্তর ইউরোপের লোক প্রোটেস্টান্ট, গোঁড়া নিরাকারবাদী, ওদের চিত্রকলা একান্ত দরিদ্র, ভাস্কর্যের বালাই ওদের নেই। ওরা মুসলমান, এরা হিন্দু। ওদের তেজ বেশি, এদের লাবণ্য বেশি।
এখন বলি পারির থিয়েটারগুলির কথা। প্রথমত, পারির থিয়েটারগুলি অসম্ভব সস্তা। দ্বিতীয়ত, তাদের আয়োজন অসম্ভব জাঁকালো। লণ্ডনে যত খরচ করে যে-দরের সাজসজ্জা বা যে-দরের অভিনয় দেখতে পাওয়া যায় পারিতে তার সিকিভাগ খরচ করে তার চারগুণ ভালো সাজসজ্জা চারগুণ ভালো অভিনয় দেখতে পাওয়া যায়। এর একটা কারণ এই যে, ফরাসিরা ভালো জিনিসের কদর বোঝে, দলে দলে দেখতে যায়, প্রত্যেকে অল্প অল্প দিলেও সবসুদ্ধ অনেক টাকা ওঠে, ফলে প্রযোজনার খরচ পুষিয়ে যায়। এ ছাড়া গভর্নমেন্টও থিয়েটারওয়ালাদের অর্থসাহায্য করে, যদিও সাহায্য স্বরূপ ডান হাতে যা দেয় ট্যাক্স স্বরূপ বাঁ-হাতে তা ফিরিয়ে নেয় বলে থিয়েটারওয়ালাদের আক্ষেপ। তবু এটা তো অস্বীকার করা যায় না যে, গভর্নমেন্ট ডান হাতে যা দেয় ওটা মূলধনের কাজ করে ও ওর থেকে উচ্চাঙ্গের প্রযোজনার গোড়াকার খরচ জোটে।
পারির থিয়েটারগুলোর জাতিবিভাগ আছে; যেটাতে অপেরা হয় সেটাতে কেবল অপেরাই হয়, যেটাতে কমেডি হয় সেটাতে কেবল কমেডিই হয়, যেটাতে ক্লাসিক (গ্রিক নাটকের অভিনয়) হয় সেটাতে কেবল ক্লাসিকই হয়। লণ্ডনে কোনো স্থায়ী অপেরা গৃহ নেই এবং জাতিবিভাগ নেই। একটি স্থায়ী অপেরার স্কিম চলেছে, কিন্তু গভর্নমেন্ট এক পেনিও সাহায্য করবে না এবং জনসাধারণও যথা প্রয়োজন শেয়ার কিনবে কি না সন্দেহ। সুতরাং, যতদূর দেখছি লণ্ডনের ভাগ্যে আছে ভ্রাম্যমাণ অপেরার দলগুলির মধ্যে মধ্যে শুভাগমন। তাদের মধ্যে যেগুলি খাঁটি ব্রিটিশ সেগুলি গভর্নমেন্টের সাহায্য পায় না বলেই হোক কিংবা জনসাধারণের ঔদাসীন্যবশতই হোক কন্টিনেন্টাল দলগুলির কাছে মাথা তুলতে পারে না। কন্টিনেন্টাল দলগুলিতে অনেক দেশের শিল্পীরা যোগ দেয়, তাদের পেছনে অনেক দেশের টাকার জোর। পারির যেটি স্থায়ী অপেরাগৃহ সেটি পৃথিবীর বৃহত্তম রঙ্গালয়, তার পেছনে সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে, তার সাজসজ্জা বহুকালগত, তার নট-নটীরা সমাজে বিশিষ্ট সম্মান পায়, তাতে তাদের গভর্নমেন্ট অনেক টাকা ঢালে ও সেটি তাদের জাতীয় সম্পত্তি*। অথচ তার সিটগুলি যথেষ্ট সস্তা। পারির দরিদ্রতম শ্রমিকও তার নিম্নতম শ্রেণির দাম জোটাতে পারে। ধনী দরিদ্র সকলেরই জন্যে শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা মহার্ঘ বেশভূষা পরে মহৈশ্বর্যময় স্টেজে অবতীর্ণ হন। পারির অন্যান্য থিয়েটারগুলোরও প্রযোজনা খুব চমকপ্রদ, অথচ সিট আরও সস্তা; চার আনা দিয়ে তিন ঘণ্টা আমোদ উপভোগ করতে পারা যায়। তবে এটা ঠিক, লণ্ডনের সিটের আরাম পারির সিটে নেই, লণ্ডনের লোক চেয়ার ছেড়ে কাঠের বেঞ্চিতে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসতে চাইবে না। পারিতে অনেক শ্রেণির সিট আছে, অন্তত দশ-বারো শ্রেণির; কিন্তু উচ্চতম থেকে নিম্নতম অবধি অল্প দামের ক্রমান্বিত ব্যবধান চার আনার পরে ছ-আনা, ছ-আনার পরে আট আনা, এমনি করে সবচেয়ে দামি সিট হয়তো চার টাকা। লণ্ডনে কিন্তু এক টাকার পরে দু-টাকা তার পরে তিন টাকা, এমনি করে সবচেয়ে দামি সিট হয়তো পনেরো টাকা। সেইজন্যে ইংরেজরা থিয়েটারের চেয়ে সিনেমাই দেখে বেশি, গরিব লোকদের সংগতি নেই বলে তাদের রসবোধ অচরিতার্থ থেকে যায়। ইংরেজরা আর্টকে সর্বসাধারণের হাতে দেবার মতো স্বল্পব্যয়সাধ্য করতে পারেনি, (এদিকে একমাত্র সফল প্রচেষ্টা ‘Old Vic’), সেইজন্যে আর্ট এদের কাছে গঙ্গাজলের মতো ন্যাশনাল নয়। আমরাও যে গ্রামের লোককে গ্রামছাড়া করে শহরের কোণে কোণে বস্তি গড়ছি আমাদেরও ভাবা উচিত গ্রামের যাত্রা পার্বণ কথকতা থেকে ও শহরের নাট্য সংগীত ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত হয়ে তারা সমগ্র দেশকে নিরানন্দ করে তুলছে কি না। নাগরিকতার নাগপাশে জড়িয়ে ইংল্যাণ্ডের আত্মা যে একান্ত ক্লিষ্ট বোধ করছে ইংল্যাণ্ডের অসামান্য স্বাস্থ্যের আড়ালে ঢাকা পড়লেও তা সত্য। নাগরিক ইংল্যাণ্ড প্রাণবান কিন্তু অমৃতবান নয়, অজর কিন্তু অমর নয়।
ফরাসিদের আর একটা জাতীয় সম্পদ তাদের মিউজিয়ামগুলো। জগৎপ্রসিদ্ধ লুভর ছাড়া লুকশাঁবুর্গ, ত্রোকাদেরো, গিমে ইত্যাদি আরও ডজন খানেক ছোটো-বড়ো মিউজিয়াম আছে পারিতে। লুভরের ঐশ্বর্যের তুলনাই হয় না, তার আকার এত বড়ো যে সেটা একটা জাদুঘর নয় একটা জাদুপাড়া; সমস্তটি একবার চোখ বুলিয়ে দেখতে দু-দিন লেগে যায়। Venus de Milo-কে একটা স্বতন্ত্র ঘর দেওয়া হয়েছে, সে-ঘরে তার বন্ধুদের জন্যে চমৎকার বসবার বন্দোবস্ত রয়েছে, সেসব আসনে বসে যেকোনো কোণ থেকে তাকে নিরীক্ষণ করতে পারা যায়; বলা বাহুল্য যে-দিক থেকেই দেখি-না কেন সব দিক থেকেই সে সমান সুদর্শনা। তাজমহলকে যেমন বার বার নানা আলোকে দেখেও চির-অপূর্ব মনে হয়, গ্রিক ভাস্করের এই মানসী মূর্তিটিকেও তেমনি। তবে আমার ভারতবর্ষীয় চোখ নিছক রূপ দেখে তৃপ্তি পায় না, এবং বিউটিফুলের অতৃপ্তির চেয়ে সাব্লাইমের তৃপ্তিই তাকে প্রগাঢ়তর রস দেয়। সেইজন্যে ‘প্রজ্ঞা পারমিতা’-র ওপরে তার একটা পক্ষপাত আছে, সে-পক্ষপাত নিয়ে সে বিশ্বের সামনে তর্ক করতে চায় না, সেটা ভারতবর্ষীয় ধাতের পক্ষপাত।
আমাদের কালিদাস যে নীতিনিপুণ ছিলেন এহেন অপবাদ তাঁকে তাঁর শত্রুতেও দেবে না, আশা করি স্বয়ং দিঙনাগাচার্যও দেননি। সেই শিল্পীই কিনা উমাকে শেষকালে জননীরূপে না এঁকে তৃপ্তি পেলেন না। ফুলবতীর চেয়ে ফলবতী লতার প্রতি আমাদের ধাতুগত পক্ষপাত ‘উর্বশী’-র কবিকেও ‘কল্যাণী’ লিখিয়েছে। পারফেকশন নয়, পরিণতিই আমাদের প্রিয়; এবং নীতি নয় রুচিই আমাদের অন্তর্মুখীন করেছে। বিবসনা শ্যামাকে মা বলতে পারি তো বিবসনা Venus-কেও প্রিয়া বলতে পারতুম, তবু যে বলিনে এর কারণ যতই নিখুঁত হোক না-কেন Venus-এর পরিণতি নেই, বৃদ্ধি নেই। সে আমাদের শুধু একটা রসই দেয়, জীবনের সমস্ত রস দেয় না। তার মধ্যে আমাদের কুমারের জননীকে দেখিনে—‘নহ মাতা নহ কন্যা নহ বধূ সুন্দরী রূপসী।’
লুভর মিউজিয়ামে ‘মোনালিসা’-কেও (লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি-কৃত) দেখলুম। তার সেই রহস্যময় হাসি মানুষের পিছু নেয়, তাকে ভোলবার সাধ্য নেই, ইচ্ছা করলেও চেষ্টা করলেও ভুলতে পারিনে। লুভরে কিছু না-হোক লাখ খানেক ছবি তো আছেই, পৃথিবীর সেরা শিল্পীদের আঁকা। কেমন করে বলব যে তার চেয়ে কেউ সুন্দরী নয়? তখন তো মনে হচ্ছিল অনেকেই সুন্দরতরা। একে একে সকলেই মিথ্যা হয়ে গেছে স্বপ্নদৃষ্টার মতো। প্রভাতী তারার মতো চোখে লেগে আছে শুধু ‘মোনালিসা’-র হাসিটি।
ফরাসিরা এসব ছবি এসব মূর্তি নানা উপায়ে সংগ্রহ করেছে, সব উপায় সাধুও নয়। এদের অনেকগুলি যুদ্ধলব্ধ। রাজ্য জয় করে অনেক বিজেতা অনেক রত্নই হরণ করে, কিন্তু ফরাসিরা হরণ করেছে শিল্পসম্ভার। ফরাসিদের হারিয়ে দিয়ে বিসমার্ক অনেক কোটি স্বর্ণমুদ্রা আদায় করেছিলেন, সে-সোনা এতদিনে ধুলা হয়ে গেছে, জার্মানি এখন পুনর্মূষিক। কোন জাতি কোন জিনিসকে বেশি দাম দেয় তাই নিয়েই তার ইতিহাস। ভারতবর্ষ যদি আত্মাকে সত্যিই তার সর্বস্ব দিয়ে কিনে থাকে তবে ভারতবর্ষের আত্মা মরবে না।
ইংল্যাণ্ডের ব্রিটিশ মিউজিয়াম প্রভৃতি জাতীয় সম্পদ দেখে যা মনে হয়েছিল ফ্রান্সের লুভর ত্রোকাদেরো প্রভৃতি জাতীয় সম্পদ দেখে তাই মনে হল। ভাবলুম ইংল্যাণ্ডে ফ্রান্সে জন্ম নিয়ে আত্মিক সুবিধা আছে, বাল্যকাল থেকেই মিউজিয়াম দেখতে দেখতে মানুষ হব। বিশ্বমানবের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়ে সৃষ্টিরহস্য ভেদ করে, তখন যদি আর্টক্রিটিক হয়ে উঠি তো বাংলা মাসিকপত্রের মাসিক সাহিত্য সমালোচনা করতে গিয়ে রসবোধের শ্রাদ্ধ করব না, চোখ পাকবে কিন্তু মন পাকবে না, প্রতিদিন একটু করে বড়ো হব কিন্তু বুড়ো হব না, আমার প্রাচীন দেশের পরিপক্ব শিক্ষাকে আমার চিরতরুণ অন্তরে ধারণ করব এবং প্রতি দেশের নিজস্ব শিক্ষাকে আমার নিজস্ব শিক্ষার মধ্যে গ্রহণ করব।
ফরাসি জাতিটা হচ্ছে যাকে বলে কসমোপলিটান। এর মানে এ নয় যে ওরা বিশ্বপ্রেমিক, এর মানে ওরা বিশ্বচেতন। প্রমাণ ওদের পথঘাটের নামগুলো। পৃথিবীর সব দেশের ইতিহাস ও সব দেশের ভূগোল পড়বার যাঁদের সময় নেই তাঁরা কেবল পারির মানচিত্রখানার ওপরে চোখ বুলিয়ে যান, দেখবেন রাস্তার নাম লণ্ডনের মতো প্রত্যেক পাতায় একটা করে Old Street, New Street. High Street ও Park Road নয়, রাস্তার নাম Moscou, Tokio, Pekin, Constantinople ইত্যাদি ও President Wilson, Edouard VII, Garibaldi, Hausmann ইত্যাদি। প্লাসের নাম Etats-unis (ইউনাইটেড স্টেটস,) Italie, Europe ইত্যাদি ও রেলস্টেশনের নাম George V, St. Francis Xavier, Michel-Ange (মাইকেল এঞ্জেলো) ইত্যাদি। এ ছাড়া স্বদেশের মহাপুরুষ মাত্রেরই ও স্বদেশের প্রতি অংশের নাম পারির সর্বাঙ্গে বৈষ্ণবের সর্বাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামের মতো ছাপা। ফ্রান্সের লোকের দেশাত্মজ্ঞান অমনি করেই হয় বলেই তাদের দেশাত্মবোধ আপনা-আপনি জন্মায়। শৈশব থেকেই তারা পথে চলতে চেনে তাদের জাতীয় পূর্বপুরুষদের—যাদের নিয়ে তাদের ইতিহাস লেখা হয়েছে; আর দেশের প্রতি জেলার প্রতি শহরের প্রতি পর্বতের নাম—যাদের কোলে তাদের অখন্ড জাতি লালিত হয়েছে। স্বদেশকে চেনে বলেই তারা স্ববিশ্বকেও চিনতে পারে।
৭
এদেশে স্বতন্ত্র বর্ষা ঋতু নেই বলে প্রত্যেক ঋতুই অংশত বর্ষা ঋতু। সময় নেই অসময় নেই বর্ষা ঋতুর বর্গিরা অপর ঋতুদের খাজনা থেকে চৌথ আদায় করে যায়। সকাল বেলা শুয়ে শুয়ে দেখলুম আলোতে ঘর ভরে গেছে, ফুটফুটে খোকার মুখে হাসি আর ধরে না, আকাশের সেই হাসি তরুণী ধরণির মাতৃমুখখানিকে পুলকে গর্বে উজ্জ্বল করে তুলেছে। এটা বসন্তকাল। কোকিলের কুহু শুনছিনে, কিন্তু সমস্ত দিন কত পাখির কিচিমিচি। গাছেরা নতুন দিনের নতুন ফ্যাশন অনুযায়ী সাজ বদলে ফেলেছে, তাদের এই কাঁচা সবুজ রঙের ফ্রকটিকে তারা নানা ছলে দেখাচ্ছে, ঘুরে ফিরে দেখাচ্ছে, আধেক খুলে দেখাচ্ছে। বাতাস একজন গ্যালান্ট যুবার মতো তাদের শ্রীমুখের তুচ্ছতম মামুলিতম কায়দাদুরস্ত ফরমাশ শুনবে বলে উৎকর্ণ হয়ে নিমেষ গুনছে এবং শুনবামাত্র শশব্যস্ত হয়ে দিগ্বিদিক ছুটে বেড়াচ্ছে। তার সেই ব্যস্ততার উষ্ণ স্পর্শ পেয়ে উঠে বসলুম। ভাবলুম এবারকার বসন্তটাকে এক ফার্দিং-ও ফাঁকি দেব না, পরিপূর্ণভাবে ভোগ করে নেব। আকাশ এত নীল, মাটি এত সবুজ, বাতাস এত কবোষ্ণ, পাখি এত অস্থির, ফুল এত অজস্র—এই ভরা ভোগের মাঝখানে আমি যদি আনমনা থাকি তো আমার শিরশি চতুরানন কী না লিখবেন?
কিন্তু, এ কী হা হন্ত কোথা বসন্ত! দেখতে দেখতে এলেন কিনা ইন্দ্ররাজের ঐরাবতের পাল, স্বর্গরাজ্যের স্কুলমাস্টার তাঁরা, অত্যন্ত পক্ব প্রবীণ অভ্রান্ত তাঁদের গুম্ফশ্মশ্রু-ধবল বদনমন্ডল। তাঁদের স্থূল হস্তাবলেপনে আকাশের চোখ ফেটে জল পড়তে লাগল, তার সদ্যোজাত লাবণ্য গেল এক ধমকে মলিন হয়ে। হায় হায় করে উঠল পৃথিবীর জননী-হৃদয়টা।
এদেশের এই খেয়ালি ওয়েদার দু-দিনেই মানুষকে মরিয়া করে তোলবার পক্ষে যথেষ্ট। বার বার আশাভঙ্গের মতো পরীক্ষা আর নেই, প্রতিদিন সেই একই পরীক্ষা। সকালের আশা দুপুরে ভাঙে, রাত্রের আশা সকালে ভাঙে। নিত্য অনিশ্চয়ের মধ্যে বাস করতে করতে জীবনের ফিলসফিটাই যায় বদলে। মনে হয়, দূর হোক ছাই, বাইরের কাছ থেকে খুব বেশি প্রত্যাশা করব না, কালেভদ্রে যখন যেটুকু পাই তখন সেইটুকুকেই হাতে হাতে ভোগ করে নিতে প্রস্তুত থাকি, অন্যমনস্কভাবে লগ্ন না বইয়ে দিই, কিংবা চপল লগ্নকে রয়ে-সয়ে ভোগ করতে গিয়ে মুখের গ্রাস থেকে বঞ্চিত না হই।
বাইরের কাছ থেকে আনুকূল্য না পেয়ে ইংল্যাণ্ড একদিকে হয়েছে ভোগগ্রাহী, অন্য দিকে হয়েছে ভোগসংগ্রাহী। সে বাইরে থেকে যা পায় তার তলানি অবধি শুষে নেয়, যা পায় না তাকে প্রাণপণে অর্জন করে। বার বার আশাভঙ্গজনিত অনিশ্চয়তাকে অভিভূত করতে পারলে সে কবে মরত, কিন্তু ওতে তাকে অভিভূত করা দূরে থাক, তার জেদ বাড়িয়ে দিয়েছে। বাইরের সঙ্গে তার যে পরিচয় সে যেন ‘খড়্গে খড়্গে ভীম পরিচয়।’ প্রতিপক্ষকে হার মানাবে বলে সে প্রতিপক্ষের নাড়িনক্ষত্র জেনে নিয়েছে—সেই হচ্ছে তার বিজ্ঞান। জগৎটাকে মায়া বলবার মতো সাহস যে তার হয়নি তার কারণ মরীচিকা দেখতে পাবার মতো চোখ-ধাঁধানো সূর্যালোক এদেশে দুর্লভ। যা পায় তাকে অনিত্য বলে ত্যাগ করবার মতো বাবুয়ানাও তার সাজে না, কেননা সে যা পায় তা অপ্রসন্না প্রকৃতির বাম হস্তের মুষ্টিভিক্ষা, আর আমরা যা পাই তা অন্নপূর্ণা প্রকৃতির অঞ্জলিভরা দান। ভিক্ষা করে এদেশে একমুঠো ভিক্ষার সঙ্গে এক মুঠো অপমান মেলে যে, নিতান্ত দায়ে ঠেকলে ভিক্ষার চেয়ে উদবন্ধনই হয় শ্রেয়। অথচ ভিক্ষা করাটা আমাদের উপনয়নের অঙ্গ, সন্ন্যাসের অবলম্বন, আমাদের শিব স্বয়ং ভিখারি। অবশেষে এমন দাঁড়িয়েছে যে, আমাদের দেশে সন্ন্যাসী যত আছে গৃহস্থ তত নেই, মুখের চেয়ে হাতের সংখ্যা কম, পুরুষকারের অভাবে দেশজোড়া ক্লৈব্য। সেইজন্য ভোগের নামটা পর্যন্ত আমাদের কানে অশ্লীল।
ইংল্যাণ্ডের মানুষের একমাত্র ভাবনা সে জীবনটাকে এনজয় করতে পারছে কি না; এনজয় করা ছাড়া তার কাছে জীবনের অন্য কোনো মানে নেই। ভোগের জন্যে সে প্রাণপণে ভুগেছে, বার বার আশাভঙ্গ সত্ত্বেও প্রাণ ভরে আশা রেখেছে, যে-লক্ষ্মীকে সে অর্জন করল তাকে যদি সে ভোগ করতে না পারল তবে তার জীবনটাই ব্যর্থ হল। তার স্ত্রীকে তো সে পিতার হাত থেকে পায়নি যে অতি সহজে ত্যাগ করে সন্ন্যাসীয়ানা করবে! সে স্বয়ংবর সভার বীর, প্রকৃতি তার ভোগ্যা। প্রকৃতিকে এড়াবার তপস্যা তার নয়—মুক্তি নয়, ভুক্তিই তার লক্ষ্য; এর জন্যে যে-ক্ষমতা চাই সেই ক্ষমতার তপস্যাই ইংল্যাণ্ডের তপস্যা।
ইস্টারের ছুটিতে লণ্ডনের বাইরে গিয়ে ভোগের চেহারা দেখলুম। তপস্যার জন্যে কাজের জন্যে লণ্ডন! ভোগের জন্যে ছুটির জন্যে সমস্ত ইংল্যাণ্ড। যেখানে যাই সেখানে দেখি অসংখ্য হোটেল, বোর্ডিং হাউস, সরাই, রেস্তরাঁ; পেয়িং গেস্ট রাখতে ইচ্ছুক গৃহস্থবাড়ি। সর্বত্র মোটরগম্য মজবুত তকতকে রাস্তা। সমুদ্রতীরবর্তী স্থানগুলিতে স্নান, সাঁতার, নৌচালনার আয়োজন। কোথাও মাছধরা, কোথাও শিকার-করা। সর্বত্র টেনিস কোর্ট, সর্বত্র গলফ কোর্স। এমন স্থান অতি অল্পই আছে যেখানে সিনেমা নেই, টেলিগ্রাফ-টেলিফোন-ডাকঘর নেই, সারকুলেটিং লাইব্রেরি নেই। যার যতদূর সাধ্য সে ততদূর খরচ করে ছুটি কাটাতে যায়, অত্যন্ত স্বল্পবিত্তদের পক্ষেও এর ব্যতিক্রম হয় না। আমাদের যেমন তীর্থযাত্রার বাতিক, এদের তেমনি হলিডে হ্যাবিট। কাজের সময় যেমন কাজকে এক মিনিট ফাঁকি দেয় না, ছুটির সময় তেমনি ছুটিকে এক সেকেণ্ড ফাঁকি দেয় না। ছুটি পেলেই এক-একখানা সুটকেস হাতে করে বালকবৃদ্ধবনিতা কর্মস্থল ছেড়ে ক্রীড়াস্থলে রওয়ানা হয়। তারপর একস্থানে যতদিন খুশি হোটেলবাস, char-a-banc পূর্বক স্থান পরিক্রমা, খেলাধুলার ধুম, পানাহারের আড়ম্বর, নাচ-গানের মজলিশ। গত যুগের পূজাপার্বণ আর নেই, দেড় শতাব্দীর ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন ইংল্যাণ্ডের চেহারা বদলে দিয়েছে। কর্মের সঙ্গে ধর্মের এবং ছুটির সঙ্গে পার্বণের যে সোদর সম্বন্ধ ছিল এখন সে-সম্বন্ধ অনেক দূর সম্বন্ধ, মাঝখানে অনেক পুরুষ গত হয়েছে।
আমি যে-অঞ্চলে গিয়েছিলুম তার নাম আইল অব ওয়াইট। দ্বীপটির পরিধি প্রায় ৬০ মাইল, কিন্তু তারই মধ্যে গুটি আট-দশ ছোটো ছোটো শহর ও বিশ-পঁচিশটি ছোটো ছোটো গ্রাম। এই শহর ও গ্রামগুলির অধিকাংশই টুরিস্টজীবী। গ্রীষ্মকালে যেসব টুরিস্ট আসে তাদের খাইয়ে খেলিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাদেরই দৌলতে বৎসরের বাকি সময়টা নিশ্চিন্তে ঘুমোয়। তখন হোটেলগুলো খাঁ-খাঁ করতে থাকে, দোকানপাট কোনোমতে বেঁচেবর্তে রয়, খেলার মাঠে আগাছা গজায়। স্থানীয় লোকগুলি সাধারণত চাষা-মুদি-রুটিনির্মাতা-মাঝি-জেলে-মজুর। তবু এরাই নিজেদের প্রতিনিধি দিয়ে এইসব শহর গ্রাম শাসন করে। খুব ছোটো ছোটো গ্রামগুলিতেও স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত।
শহর যেমন সব দেশেই প্রায় একইরকম, গ্রামও দেখলুম সব দেশেই প্রায় একরকম। মুক্ত প্রকৃতির মাঝখানে ইট-পাথরের দেয়ালের ওপরে খড়ের চালা বা টালির ছাদ, দেয়ালের গায়ে লতা উঠেছে, ছাদের উপর ঘাস গজিয়েছে—এরই নাম কটেজ। তবে নতুনের সঙ্গে সন্ধি না করে পুরাতনের গতি নেই। সংকীর্ণ গবাক্ষ কিন্তু কাচের শার্সি, সেকেলে গড়ন কিন্তু একেলে সরঞ্জাম। মুদির দোকানে ডাকঘর বসেছে, তামাক-চকোলেটের দোকানে টেলিফোনের আড্ডা, রেলস্টেশনের ভিতরে সস্ত্রীক স্টেশনমাস্টারের আস্তানা। প্রত্যেক গ্রামে ছেলেদের খেলার মাঠ আছে, পাবলিক লাইব্রেরি আছে। স্কুলের চেয়েও এ দুটো জিনিস উপকারী। স্কুলের সংখ্যা কমে এ দুটোর সংখ্যা বাড়লে ছেলেগুলি বাঁচে। শিক্ষার নামে শিশুমনের ওপর যে-বলাৎকার সব দেশেই চলে এসেছে এ যুগের শিশু সে-বলাৎকার সহ্য করবে না। শিশুও চায় স্বরাজ। তার নিজস্ব শিক্ষা সে নিজেই খুঁজে নেবে।
শহর ও গ্রামগুলি যেমন পরিষ্কার তেমনি পরিপাটি। ক্ষুদ্রতম গ্রামেরও পথঘাট অনবদ্য এবং বাড়িঘর সুখদৃশ্য। অতি দরিদ্র ঝাড়ুদার (চিমনি-সুইপ) যে-বাড়িতে থাকে সে-বাড়ির বাইরে বেল আছে, তার কাচের জানালার ওপাশে ধবধবে পর্দা, যথাস্থানে সন্নিবেশিত অল্পবিস্তর আসবাব; সমস্ত গৃহটির বাইরে-ভিতরে এমন একটি শৃঙ্খলা ও পারিপাট্যের আভাস যে তেমনটি আমাদের ধনীদের গৃহেও বিরল। ধন নয়, মনই রয়েছে এর পিছনে; সে-মন ভোগ-তৎপর মন। সেটি যদি থাকে তো উপকরণের অভাব হয় না; যা জোটে তাকেই কাজে লাগানো যায়, যা জোটে না তাকে অর্জন করে নেওয়া যায়। এ সংকেত আমরা জানিনে, কেননা পরলোকে বাসা বাঁধবার ব্যস্ততায় ইহলোকের বাসাকে আমরা এক রাত্রির পান্থশালা ভেবে এসেছি, তার প্রতি আমাদের দায়িত্ব মানিনি। যে-দেহে বাস করি সে-দেহকে যেমন অনিত্য ভেবে অনাস্থা দেখাই, যে-গৃহে বাস করি সে-গৃহকেও তেমনি অনিত্য ভেবে অবহেলা করি। এদিকে কিন্তু ইহলোককে এরা মরেও ছাড়তে চায় না, কফিনের ভিতরে শুয়ে মাটিকে আঁকড়ে ধরে। এদের বিশ্বাস জগতের শেষ দিন অবধি এদের এই মাটির শরীরখানা থাকবে।
তা ছাড়া আমার মনে হয় এ দেশের এই গৃহ-পারিপাট্য ও পরিচ্ছদ-পারিপাট্যের মূলে রয়েছে এদেশের নারীশক্তির সক্রিয়তা। আমাদের ইহবিমুখ ধর্ম হচ্ছে নারীবিমুখ ধর্ম, আমাদের একান্নবর্তী পরিবারে নারীর অন্তরের সায় নেই, আমাদের গৃহ নারীর সৃষ্টি নয় এবং গৃহের বাইরেও নারী আমাদের সৃষ্টি করতে পায় না। ইংল্যাণ্ডের নারী তার স্বামীগৃহের রানি, শাশুড়ি জা-দের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নেই, নিজের ঘরের সমস্ত দায়িত্ব এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তার হাতে, সেইজন্যে ইংল্যাণ্ডের গৃহিণীর হাত এক মুহূর্ত বিশ্রাম পায় না, ঘরটির ঝাড়া-মোছা ঘষা-মাজাতে সর্বক্ষণ ব্যাপৃত। সন্তান সম্বন্ধেও ঠিক তেমনি দায়িত্ব এবং ততখানি স্বাধীনতা। জা শাশুড়ির সাহায্য নেই হস্তক্ষেপ নেই। ইংল্যাণ্ডের ছেলেরা ‘হোম’ নামক যে-জিনিসটি পায় সেটির একদিকে মা অন্যদিকে বাবা, মাঝখানে ছোটো-বড়ো ভাইবোনগুলি। সকালে-দুপুরে-সন্ধ্যায় এক টেবিলে সকল ক-টিতে মিলে খায়, রাত্রে এক অগ্নিস্থলে সকল ক-টিতে মিলে গল্প বা গান-বাজনা করে; অল্পে সম্পূর্ণ ছোটো একটুখানি নীড়। এর মধ্যে শৃঙ্খলারক্ষা সহজ, এর মধ্যে দায়িত্ব ভাগাভাগি করতে গিয়ে নিত্য কলহ নেই, এটা একটা বিরাট যজ্ঞশালার মতো কোলাহলমুখর নয়।
সে যা-ই হোক, ইংল্যাণ্ডের গৃহিণীদের কাছ থেকে আমাদের গৃহিণীদের অন্তত একটি বিষয় ভক্তিভরে শিক্ষা করবার আছে, সেটি গৃহের শৃঙ্খলাবিধান ও পারিপাট্যসাধন। নিজের আশপাশকে নিয়েই নারীর সৃষ্টি। নারীর আভামন্ডল হচ্ছে নারীর পরিচ্ছদ, নারীর গৃহ। কিন্তু আমাদের রন্ধনপর্ব এত অধিক সময় নেয় যে, তারপরে অন্য কিছু করবার না-থাকে অবসর না-থাকে বল। অথচ গ্যাসের উনুনের সাহায্যে এদেশে দরিদ্রতমা গৃহিণীরাও আধ ঘণ্টায় এক বেলার রান্না চুকিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত। তারপরে হায়ার পারচেজ প্রথার প্রবর্তন হয়ে অবধি গরিবের ঘরের আসবাবের নিঃস্বতা নেই, অনেকের একটি পিয়ানো পর্যন্ত আছে। কোন বিষয়ে খরচ কমিয়ে কোন বিষয়ে খরচ বাড়াতে হয় সেটা একটা আর্ট। খরচ কমানো মানে কেবল টাকার খরচ না, সময়েরও খরচ। আমাদের দেশে যা দাসীর কাজ এদেশের গৃহিণীরাও তা যন্ত্রের সাহায্যে সংক্ষিপ্ত করে স্বহস্তে সারেন। তার ফলে যে-টাকা ও সময় বাঁচে সে-টাকায় ও সময়ে বিদ্যাবতী-কলাবতী-স্বাস্থ্যবতী হওয়া যায়। গ্রামে দেখলুম প্রায় প্রত্যেকেরই বাগান আছে; সে-বাগানে বাড়ির মেয়েরাই কাজ করে, ছেলেরা বাইরের কাজে ব্যস্ত। লণ্ডনেও অনেক বাড়িতে ছোটো একটুখানি বাগান আছে, বাগানকে ইংরেজরা বড়ো ভালোবাসে। বাইরের কাজ থেকে ফিরে এসে বাগানের কাজ করা এদের অনেকেরই একটা হবি। গ্রামে দেখলুম অবসর পেলেই গৃহিণীরা সেলাই নিয়ে বসেছেন, গল্পগুজবে গা ঢেলে দিয়েও হাতের কাজটিতে ঢিলে দিচ্ছেন না। হাজারো বিলাসিতা করুক, এদেশের মেয়েরা উপার্জন করতে পটু, তথা উপার্জন বাঁচাতেও পটু। গ্রামের মেয়েদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয় কারুশিল্পের ও গার্হস্থ্য অর্থনীতির। জনপিছু ছ-পেনি খরচ করে কতখানি সাপার (নৈশ ভোজন) রাঁধা যেতে পারে কিংবা অল্প খরচে কী কী পোশাক স্বহস্তে তৈরি করা যেতে পারে—প্রতিযোগিতার এইরূপ বিষয় নির্দেশ করে দেন গ্রামের কর্তৃপক্ষ। অনেক বাড়িতে যে বাগান আছে সেই বাগানে পর্যটকদের চা খাইয়ে অনেকে সংসারের আয় বাড়ায়। এইসব ‘টি-গার্ডেন’ ছাড়া অনেকের বাড়িতে বা ফার্ম হাউসে দু-তিনটে ঘর খালি থাকে, সেখানে পেয়িং গেস্ট রাখা হয়। অধিকাংশ গৃহস্থের মুরগি শুয়োর গোরু ইত্যাদি প্রয়োজনীয় পোষ্য আছে। অর্থাগমের ও অর্থ সঞ্চয়ের যত উপায় আছে কোনোটাই কেউ পারতপক্ষে বাদ দেয় না।
গ্রামে দেখলুম সাইকেলের চল কিছু বেশি, এবং ওটা সাধারণত মেয়েদেরই যান। মেয়েরা ওই চড়ে বাজার করতে যায়। ছেলেরা চড়ে মোটর সাইকেল। তবে মেয়েরা যেমন উঠেপড়ে লেগেছে আর-কিছুকাল পরে ওটাও হবে প্রধানত মেয়েলি যান। এরোপ্লেনে করে আটলান্টিক অতিক্রম করতে গিয়ে মরাটাই হচ্ছে এখন তাদের আধুনিকতম ফ্যাশন। হিস্টিরিয়ায় মরার চেয়ে এটা তবু স্বাস্থ্যকর ফ্যাশন। মহাযুদ্ধের পর থেকে ইউরোপে cult of joy-এর চর্চা বেড়েছে। যুবকরা জেনেছে যেকোনো দিন দেশের ডাকে প্রাণ দিতে হবে, এই নিষ্ঠুর যুগে প্রাণের মূল্য নেই, প্রাণ সম্বন্ধে সিরিয়াস কেউ নয়। সুতরাং যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আস। যুবতীরা জেনেছে পুরুষসংখ্যার স্বল্পতাবশত বিবাহ অনেকের ভাগ্যে নেই, আর্থিক অসচ্ছলতাবশত মাতৃত্ব আরও অনেকের ভাগ্যে নেই। সুতরাং, যতটুকু পাই হেসে লব তাই। ঘোরতর মোহভঙ্গের ভিতরে এ যুগের তরুণ-তরুণীরা বাস করছে। ছেলেদের চোখে ডেমোক্রেসির কালো দিকটা ধরা পড়ে গেছে, ঊনবিংশ শতাব্দীর সব আদর্শ খেলো হয়ে গেছে। জীবন নামক চিত্রিত পর্দাখানা তারা তুলে দেখছে এর পেছনে লক্ষ্য বলে কিছু নেই—শুধু বাঁচবার আনন্দে বাঁচতে হবে, হাসবার আনন্দে হাসতে হবে। এ যুগের তরুণ যত হাসে তত ভাবে না। মেয়েরা বুঝতে পেরেছে ভোট এবং আর্থিক অনধীনতাই সব কথা নয়, ওসব পেয়েও যা বাকি থাকে তার ওপরে জোর খাটে না, সেটা হচ্ছে পরের হৃদয়। এ যুগের মেয়েদের মতো দুঃখিনী আর নেই। তবু তারা পণ করেছে কিছুতেই কাঁদবে না, কিছুতেই হটবে না। জীবনের কাছ থেকে খুব বেশি প্রত্যাশা করা চলে না, এইটে এ যুগের ইউরোপের মূল সুর। যেটুকু আমাদের নিজেদের আয়ত্তগম্য সেইটুকুর ওপরে এ যুগের ইউরোপের ঝোঁক পড়েছে। সেইজন্যে এত দেহের দিকে নজর, যৌবনের দিকে নজর। ক্রমশই ইউরোপের লোকের স্বাস্থ্য বেড়ে চলেছে, আয়ু বেড়ে চলেছে, যৌবন বেড়ে চলেছে। সেই গর্বে এ যুগের অগ্রসরপন্থীরা খ্রিস্টীয় চরিত্রনীতি মানতে চায় না, ইউরোপে এখন পেগানিজমের যুগ ফিরে এসেছে, দেহের উৎকর্ষের জন্যে এখন চরিত্রের সাতখুন মাপ।
এ যুগের মানুষ নির্জনতাকে বাঘের মতো ডরায়, গ্রামের আদিম নির্জনতার ভয়েই সে শহর শরণ করেছে। শহরে অরুচি হলে মাঝে মাঝে মুখ বদলাবার জন্যে সে গ্রামে যায়, সেইসঙ্গে শহরে আমোদপ্রমোদ আরাম বিলাসগুলোকেও পুটলি বেঁধে গ্রামে নিয়ে যায়। প্রতি গ্রামের যে একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল নাগরিক সভ্যতার স্টিম রোলার তাকে থেঁতলে গুঁড়িয়ে সমতল করে দিচ্ছে। সেই সমতলের ওপর দিয়ে নাগরিকের দল char-a-banc চড়ে দু-ঘণ্টায় ষাট মাইল চক্কর দিয়ে যান, তারই নাম দেশভ্রমণ। এবং ছেঁটে কেটে সমান করে আনা দৃশ্যগুলোকে মুহূর্তমাত্র চোখে ছুঁইয়ে পরমুহূর্তে বিস্মৃতিরওয়েস্ট পেপার বাস্কেটের মধ্যে নিক্ষেপ করেন, তারই নাম দেশ দর্শন। তারপর সন্ধ্যা জুড়ে বন্ধ ঘরে সিগরেটের ধোঁয়ায় অন্ধকূপ রচনা করে সেই গর্তের মধ্যে সিনেমা দেখা এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আহার-নিদ্রা-বিশ্রম্ভালাপ। কাজের দিনে ভূতের মতো খাটুনি, ছুটির দিনে অরসিকের মতো সময়ক্ষেপ।
শহরে এ জিনিস চোখে লাগে না, কিন্তু গ্রামে যখন এই জিনিস দেখি তখন কেমন খাপছাড়া ঠেকে, চারিদিকের সঙ্গে এর মেলে না। প্রকৃতি সেই আদিকালের মতো শান্ত সুস্থির আত্মস্থভাবে কাজের সঙ্গে ছুটির মিতালি করে গরজের সঙ্গে আনন্দের তাল রেখে একঠাঁই দাঁড়িয়ে একটি পায়ে নূপুর বাজাচ্ছে। আর মানুষ কিনা কাজকে দাসখত লিখে দিয়ে তার অনুগ্রহদত্ত অবকাশটুকু লাটিমের মতো ঘুরে অপচয় করছে। সমুদ্রের কলরোলের দিকে কান দেবার অবসর নেই, তৃণের সীমাহীন শ্যামলতার আহ্বানে চোখ সাড়া দেয় না। মাথার ওপরে উড়ছে এরোপ্লেন, সমুদ্রের ওপরে ভাসছে লাইনার জাহাজ, রাস্তা তোলপাড় করছে বাস মোটর, মাঠ তোলপাড় করছেন গলফ ক্রীড়ারত টেনিস ক্রীড়ারত মানব-মানবীর দল। গতিশীল সভ্যতা যে জীবনের আনন্দ বাড়িয়েছে এমন তো মনে হয় না, বাড়িয়েছে কেবল জীবনের উত্তেজনা। জীবনকে সচেতনভাবে ভোগ করা নয়, কোনোমতে হেসে-খেলে ভুলে কাটিয়ে দেওয়া। নির্জনতার মধ্যে নিজের সঙ্গে একলা থাকার মতো শাস্তি আর নেই। কাজে হোক অকাজে হোক কিছু-একটাতে ব্যাপৃত না থাকতে পারলে মনে হয় সময়টা মাটি হল, এই সময়টা অন্যেরা কাজে লাগাচ্ছে, ফুর্তি লুটছে। কাজের দিনে এক মুহূর্ত ধ্যানস্থ হবার জন্যে স্থির হবার জো নেই পাছে প্রতিযোগীর দল মাড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে যায়, পেছিয়ে পড়ে প্রাণে মরি। ছুটে চলার এই বেগ ছুটির দিনেও সংবরণ করতে পারিনে, নানা ব্যসনে নিজেকে ব্যস্ত রেখে মনে করি খুব এনজয় করছি বটে, এই তো সক্রিয় আনন্দ, এই তো জ্যান্ত মানুষের মতো। আসলে কিন্তু এইটেই হচ্ছে চূড়ান্ত নিষ্ক্রিয়তা। ঢেউয়ের সঙ্গে ভেসে চলার চেয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ঢেউ ভাঙা বড়ো কঠিন আনন্দ। আত্মস্থ না হয়ে ভোগ নেই।
তবে এই একটা মস্ত কথা যে, একালের ব্যসন সেকালের মতো বলক্ষয়ী নয়। একালের মানুষ হয়তো দৃশ্য-গন্ধ-সংগীতের রসগ্রাহী নয়, কলার নামে কৃত্রিমতাকেই সে মহামূল্য মনে করে, বাস্তবতার অন্বেষণে সে কল্পনাবৃত্তি খুইয়েছে, প্রগাঢ় প্যাশনের পরিবর্তে উগ্র সেনসেশনই তার অনুভূতি জুড়েছে। তবু এসব সত্ত্বেও সে স্বাস্থ্যবান প্রাণবান বলবান। বিষপান করেও সে নীলকন্ঠ, প্রচুর হাস্যরস তার স্বাস্থ্য বাড়িয়ে দিচ্ছে, অজস্র খেলাধুলা তার বল বাড়িয়ে দিচ্ছে, বিজ্ঞান তাকে আশ্বাস দিয়ে বলছে—‘অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।’
আইল অব ওয়াইট বড়ো সুন্দর স্থান। নীল রঙের ফ্রেমে-বাঁধানো একখানি সবুজ ছবির মতো সুন্দর। তবে এদেশের সবুজ যেন আমাদের সবুজের মতো কান্ত নয়, স্নিগ্ধ নয়, কেমন যেন তীব্র আর ঝাঁঝালো। তৃপ্তি দেয় না, উন্মাদনা দেয়; ছাড়তে চায় না, টেনে রাখে; আবেশের চেয়ে জ্বালা বেশি। দ্বীপটির কোনো কোনো স্থল এত নিরালা যে নেশার মতো লাগে। দিন যেদিন উজ্জ্বল থাকে চোখ সেদিন তন্দ্রালসে নুয়ে পড়তে চায়। বাতাসে পাল তুলে দিয়ে নৌকা ভেসে যাচ্ছে। গম্ভীরভাবে ওপারের পাশ দিয়ে যাচ্ছে দূরদেশগামী জাহাজ। মাথার ওপরে চিলের মতো উড়ছে এরোপ্লেন—এত ওপরে যে তার বিকট কন্ঠস্বর কানে পৌঁছোয় না। কানে বাজছে শুধু জলকন্ঠের ছলাৎ ছল ছলাৎ ছল ছলাৎ ছল। তটকে যেন আদিকাল থেকে সেধে আসছে, তবু তার মান ভাঙাতে পারছে না। মাটি তার সবুজ চুল এলিয়ে দিয়েছে, যেমন তার রূপ তেমনি তার গন্ধ—ঘুমের থেকে প্রশান্তি কেড়ে নেয়, চেতনার থেকে প্রতীতি কেড়ে নেয়। সব মিলিয়ে মনে হতে থাকে—স্বপ্ন না মায়া না মতিভ্রম! সত্য কেবল ওই আপনভোলা শিশুগুলি, ওই যারা বালি দিয়ে ঘর তৈরি করছে, বাঁধ তৈরি করছে, ঘরের মধ্যে ভালোবাসার পুতুলকে রাখছে। সমুদ্রের এক ঢেউ এসে সব ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ওরা তাই দেখে হো-হো করে হেসে উঠছে, আবার সেই ঘর ইত্যাদি।
গ্রামের লোকগুলিকে ভালো লাগল। বিদেশি দেখলেই সম্মান করে কুশল প্রশ্ন করে, সাহায্য করতে ছুটে আসে। শহুরে ইংরেজদের দেখে ইংরেজ জাতিকে যতটা নিঃশব্দপ্রকৃতি ভেবেছিলুম গ্রাম্য ইংরেজদের দেখে ততটা মনে হল না। সৌজন্যের চেয়ে বড়ো জিনিস সৌহার্দ্য। গ্রামের লোকের কাছে অল্পেতেই ও-জিনিস পাওয়া যায়। শহরের লোকের সঙ্গে বিনা ইনট্রোডাকশনে ভাব করবার উপায় নেই, যেটুকু আলাপ হয় সেটুকু ঘড়ির উপরে চোখ রেখে। কিন্তু গ্রামের লোকের হাতে কাল অন্তহীন। সময়কে তারা ফাঁকি দিতে ডরায় না, সময়ের মূল্য নামক কুসংস্কারটা তাদের তেমন জানা নেই। তাদের নিজেদের মধ্যে পরস্পরের মনের অন্তরঙ্গতা যেমন সব দেশে, তেমনি এদেশেও। নিজের গ্রামের যেকোনো লোকের সঙ্গে দেখা হলেই নমস্কার বিনিময়, সুখ-দুঃখের আলোচনা। মুখ গুঁজে না দেখার ভান করে পালাবার পথ খোঁজা নেই, কিংবা ওয়েদার সম্বন্ধে দুটো তুচ্ছ প্রশ্নোত্তর করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চুপ করে এক গাড়িতে ভ্রমণ করা নেই।
তবে গ্রাম্য সভ্যতার এখন দিন ঘনিয়ে এসেছে সব দেশে। ইংল্যাণ্ডে এখন পল্লিতে যত লোক থাকে তার তিন গুণ থাকে নগরে। ফ্রান্সে জার্মানিতেও ক্রমশ গ্রামকে শোষণ করে নগর মোটা হচ্ছে। Back to the village যে ভারতবর্ষে সম্ভব হবে এমন তো মনে হয় না। বড়োজোর গ্রাম থাকবে দেহে, তার আত্মা যাবে বদলে। গ্রাম্য সভ্যতার শবখানাতে ভর করবে নাগরিক সভ্যতার তালবেতাল। গ্রামগুলি হবে নগরেরই খুদে সংস্করণ। তা ছাড়া গ্রামে-নগরে ভেদরেখা কোনখানে টানব? লোকসংখ্যা বাড়লেই গ্রামের নাম হচ্ছে নগর। নগরে ও গ্রামে যে প্রভেদ সেটা আকৃতিগত নয়, আকারগত প্রভেদ। নগরেরই মতো গ্রামও হোটেলে ভরে যাচ্ছে, ভাড়াঘরে ভরে যাচ্ছে। এর মানে এই যে, এ যুগের মানুষ কোথাও স্থায়ী হতে চায় না। বেদেরা তাঁবু ঘাড়ে করে বেড়ায়, আমরা তা করিনে। অন্যলোক আমাদের জন্যে তাঁবু খাটিয়ে রাখে, সারাজীবন আমরা কেবল এক তাঁবু থেকে আরেক তাঁবুতে পাড়ি দিতে থাকি। এককালে আমরা যাযাবর ছিলুম, তারপর কোনো একদিন ধানের খেতের ডাকে ঘর গড়লুম, স্থিতিশীল হলুম। এখন আমরা বাণিজ্যের পণ্য নিয়ে ফেরিওয়ালার মতো পথে বেরিয়ে পড়েছি, আমরা গতিশীল। পথও মনোহর, এতে শীত-আতপের কষ্ট আছে ধুলো-বালির ঝড় আছে, কোথাও কর্দম কোথাও কঙ্কর, তবু এও ভালো।
লণ্ডনের বাইরে গিয়ে দেখলুম লণ্ডনের জনতার ভিড়কে অন্যমনস্কভাবে ভালোবেসে ফেলেছি। কাউকে চিনিনে তবু সকলের প্রতি অজ্ঞাত টান। যেখানে যাই সেখানে দেখি লণ্ডনের লোক পরস্পরকে ঠিক চিনে নিচ্ছে। লণ্ডনে থাকলে যার সঙ্গে কোনোদিন নমস্কার বিনিময়টা পর্যন্ত হয়ে উঠত না, তার সঙ্গে অল্পেতেই ঘনিষ্ঠতা জন্মে যাচ্ছে। শহরের আড়ষ্টতা বাইরে থাকে না, আদবকায়দা চুলোয় যায়। শহর ছেড়ে যারা গেছে তাদের সেই অল্প কজনের মধ্যে কতকটা পারিবারিক সম্বন্ধের মতো দাঁড়ায়। তবে এটা দীর্ঘকালের নয় বলেই এত মধুর। সকলেই মনে মনে জানে যে, ছাড়াছাড়ি যেকোনো মুহূর্তে হতে পারে। বিচ্ছেদটা অনিশ্চিত নয়, মিলনটাই অনিশ্চিত। অবুঝের মতো ভাবতে ইচ্ছা করে, বলেও বসা যায় যে আবার দেখা হবে, পুনর্দর্শনায় চ। কিন্তু আঁধার রাতের অপার সমুদ্রের জাহাজ দুটির সেই যে সংকেত বিনিময়, সেই আরম্ভ সেই শেষ। তারপর মাথা খুঁড়লেও আর দেখা হবে না। যদি হয়ও তবে সে-দেখা বন্দরের সহস্র জাহাজের ভিড়ে। তখন জনতার টানে টানছে, জলের টান গায়ে লাগে না। তখন সে-দেখায় চমক থাকে না, মামুলি মনে হয়।
এটা পুনর্যাযাবরতার যুগ, আমরা সকলকেই চাই, কাউকেই চাইনে, আমাদের আলাপী বন্ধু শত শত, কিন্তু দরদি বন্ধু একটিও নেই। আমরা বিশ্বসুদ্ধ প্রসিদ্ধ লোকের নাড়ির খবর জানি কিন্তু আমাদেরই পাড়াপড়শিদের নাম পর্যন্ত জানিনে। পাড়াপড়শি দূরে থাক, আমাদেরই ফ্ল্যাটের নীচের তলায় যারা থাকে চোখেও তাদের দেখিনি। রেল-স্টিমার-এরোপ্লেনের কল্যাণে জগৎটা তো ছোটো হয়ে গেল, কিন্তু ঘরের মানুষকে যে মনে হচ্ছে লক্ষ যোজন দূর। তবু এও সুন্দর। আমরা পথিক, আমাদের স্নেহ প্রীতি বন্ধুতার বোঝা হালকা হওয়াই তো দরকার, নইলে পদে পদে বাঁধা পড়তে পড়তে চলাই যে হবে না। একটি প্রেমে আমরা সকল প্রেমের স্বাদ পেয়েছি, সেটি চলার পথের প্রেম। এর মধ্যে আর যা-ই থাক আসক্তি নেই। আমরা নিষ্কাম ভোগী, আমরা ভোগ করি লোভ করিনে, কেননা লোভ করলে থামতে হয়, আর পথে থামাই হচ্ছে পথিকের মৃত্যু।
৮
এই ক-টি দিন সুধায় গেল ভরে। কয়েক দিন থেকে আলোর আর অবধি নেই, ভোর চারটের থেকে রাত (?) ন-টা অবধি আলো। যেদিন সূর্য থাকে সেদিন তো স্বর্গসুখ, যেদিন মেঘলা সেদিনও সুখ বড়ো কম নয়, কেবল আলো—সেও অনেকখানি। আর উত্তাপ কোনো দিন আমাদের ফাল্গুন মাসের মতো, কোনোদিন আমাদের চৈত্র মাসের মতো। আমার পক্ষে তো বেশ আরামের কিন্তু এদেশের লোকগুলি ছটফট করতে শুরু করেছে। এদের মতে এটা অকালগ্রীষ্ম। শীত বর্ষা কুয়াশা এদের গা-সওয়া হয়ে গেছে, ও নিয়ে এরা প্রতিদিন খুঁতখুঁত করে বটে কিন্তু ও-ছাড়া আর কিছু ভালোও বাসে না।
অবশ্য সাধারণের কথাই বলছি, কেননা অসাধারণেরা তো এখন কোনো দেশের বাসিন্দা নন, তাঁরা সব দেশের বাসাড়ে। তাঁরা শীতকালটা রিভিয়েরায় কাটান, বসন্তটা সুইটজারল্যাণ্ডে, গ্রীষ্মকালটা বরফের সন্ধানে কাটান, শরৎকালটা পৃথিবী পরিক্রমায়। তা বলে সাধারণরাও যে একই স্থানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেছে এমন নয়। তারাও এক শহর থেকে আরেক শহরে এবং এক দেশ থেকে আরেক দেশে বাসা বদলাতে লেগেছে। অসাধারণদের সঙ্গে তাদের তফাতটা কেবল এই যে, তাদের টান ছুটির টান নয়, কাজের টান। তবু কাজের টানে বারোমাস কেউ কর্মস্থলে কাটায় না, এক-আধ মাসের জন্যে হলেও দশ-বিশ ক্রোশ দূরে গিয়ে মুখ বদলিয়ে আসে। আর ছুটির টানে বারোমাস যাঁরা বিশ্বময় ঘুরপাক খাচ্ছেন তাঁরাও বড়ো সাবধানি পথিক, তাঁরা এজেন্সি নিয়ে বক্তৃতা দিয়ে কাগজে লিখে পাথেয় জোটান।
পাথেয় যে যেমন করেই জোটাক সকলেই একালে পথিক, কেউ একালে গৃহস্থ হতে চায় না। এই লণ্ডন শহরে কত ফরাসি ফ্যাশনজ্ঞ, জার্মান সংগীতজ্ঞ, ইটালিয়ান নৃত্যনিপুণ, রাশিয়ান পলাতক, দিনেমার চাষিদের এজেন্ট, চাটগেঁয়ে জাহাজের খালাসি, চাইনিজ কোকেন চালানদার ইত্যাদি নানা দিগদেশাগত মানুষ এক-আধ বৎসরের জন্যে বাসা বেঁধেছে। এ শহরে না পোষালে নিউ ইয়র্কে কিংবা বুয়েন্স এয়ার্সে ভাগ্যান্বেষণ করবে। এদের সামনে সারা পৃথিবী পড়ে রয়েছে, যেখানে যতদিন থাকতে পারে ততদিন থাকবে, তারপরে সুটকেস হাতে নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়বে।
রোজ এমন লোকের সঙ্গে দেখা হয় যে পৃথিবীর কোনো-না-কোনো অঞ্চলে কাটিয়ে এসেছে। কেউ জাহাজে কাজ নিয়ে হনলুলু ঘুরে এসেছে, কেউ সৈন্যদলে যোগ দিয়ে লড়ে এসেছে। রোজ এমন লোকও দেখি যে কিছু পয়সা জমাতে পারলে এখানকার ব্যবসা তুলে দিয়ে আর্জেন্টাইনায় ব্যবসা ফাঁদবে, কিংবা নিউজিল্যাণ্ডে চাকরি জোগাড় করবে। এদের কাছে পৃথিবীটা এত ছোটো বোধ হচ্ছে যে, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত যেন কলকাতা থেকে কাশী। এদের অপরাধ কী, আমারই তো এখন মনে হচ্ছে যেন ভারতবর্ষ ছোটো একটা দেশ, বম্বে কলকাতা ছোটো এক-একটা শহর। নিউ ইয়র্কের লোক জাহাজে চড়ে ছ-সাত দিনে প্যারি পৌঁছোয়, সেখানে বাড়ির লোকের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে। আর কিছুকাল পরে যখন প্যারির সঙ্গে নিউ ইয়র্কে এরোপ্লেন চলাচল সহজ হবে, তখন নিউ ইয়র্কে ডিনার খেয়ে প্যারিতে ব্রেকফাস্ট খেতে পারা যাবে, যেমন কলকাতায় ডিনার খেয়ে কাশীতে ব্রেকফাস্ট।
এর ফলে দেশে আর মানুষের মন টিকছে না, বিদেশের স্বপ্নে মন বিভোর। শনিবার হলেই চলো লণ্ডন ছেড়ে প্যারি, সেখানে রবিবারটা কাটিয়ে ফিরে এসো লণ্ডনে। পরের শনিবারে চলো বেলজিয়াম কিংবা হল্যাণ্ড। সাত দিনের ছুটি পেলে চলো জার্মানি কিংবা সুইটজারল্যাণ্ড। তিন সপ্তাহের ছুটি পেলে চলো নিউ ইয়র্ক কিংবা ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দেড় মাসের ছুটি পেলে চলো সাউথ আফ্রিকা কিংবা ইন্ডিয়া। ছ-মাসের ছুটি পেলে চলো ওয়ার্ল্ড টুরে। এগুলো অবশ্য জাহাজি যুগের মানুষের স্বপ্ন। এরোপ্লেনি যুগের মানুষ—অর্থাৎ এরোপ্লেন যখন জাহাজের মতো সস্তা ও নিরাপদ এবং সর্বত্রগামী হবে তখনকার মানুষ অফিসের ঘড়িতে ছ-টা বাজলেই ছুটবে প্যারির এরোপ্লেন ধরতে। এখন এরোপ্লেনে প্যারি পৌঁছোতে তিন ঘণ্টা লাগছে, তখন লাগবে দেড় ঘণ্টা। সুতরাং ডিনারের সময় প্যারিতে হাজির হতে পারবে। শনিবার হলে সে ভাববে যাওয়া যাক ইজিপ্টে, রবিবারটা পিরামিড দেখে সোমবার সকালে পৌঁছে ব্রেকফাস্ট খেয়ে লণ্ডনের অফিসে আসা যাবে গাধাখাটুনি (ড্রাজারি) খাটতে। খাটুনির ফাঁকে রেডিয়োতে শোনা যাবে বুয়েন্স এয়ার্সের ট্যাঙ্গো নাচের বাজনা আর টেলিভিশনে দেখা যাবে সেই নাচের দৃশ্য। ওই উত্তেজনায় আরও কিছুক্ষণ গাধাখাটুনি সুসহ হবে। তারপরে ছুটি, প্যারি গমন, রাত্রিভোজন, থিয়েটার দর্শন, নিদ্রা।
আমাদের নাতি-নাতনিরা ভাববে, এই তো জীবন! আমরাই তো সেন্ট পারসেন্ট বাঁচছি! আমাদের পূর্বপুরুষগুলো কি বাঁচতে জানত? ছিল ওদের আমলে এমন সব পাড়াময় শহরময় হোটেল? পেত ওরা এমন সব কলে তৈরি বিশুদ্ধ হাইজেনিক খাবার? পারত ওরা নিউ ইয়র্কের ব্যাণ্ড শুনতে শুনতে কলকাতায় নাচতে? সারা জগতের কোথায় কী ঘটছে তা চোখে দেখতে দেখতে বিশ্রামকাল কাটাতে? ওদের সময় নাকি স্নেহ প্রেম আতিথ্য ইত্যাদির ছড়াছড়ি ছিল—বাজে কথা। ওদের সময় গ্রামে গ্রামে মামলা-মোকদ্দমা দেশে দেশে যুদ্ধ লেগেই থাকত—ইতিহাসে লেখে। মেয়েরা নাকি গৃহকোণে বন্দি হয়ে স্বামী-পুত্রের সেবা করত—ধিক। মেয়েদের যেন নিজস্ব প্রতিভা নেই, তারা যেন পুরুষের মতো তাই নিয়ে দিনরাত ব্যাপৃত থাকতে পারে না, তাদের যেন পাবলিকের প্রতি দায়িত্ব নেই, তারা থাকবে স্বার্থপরের মতো গৃহসংসার নিয়ে!
হায়! গতি-গর্বে গর্বিত হয়ে ওরা তো বুঝবে না ওদের পূর্বপুরুষদের স্থিতিসুখ। ওরা যখন ঘণ্টায় একশো মাইল বেগে এরোপ্লেন চালিয়ে থ্রিলের আতিশয্যে মূর্ছাসুখ পাবে, তখন তো ওরা বুঝবে না গোরুর গাড়িতে চড়ে ঘণ্টায় এক মাইল অগ্রসর হবার তন্দ্রাসুখ। মার্স ভিনাসের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধাবার উত্তেজনায় ওরা ভুলে থাকবে আমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে দাঙ্গা বাঁধাবার উত্তেজনা। পৃথিবীটাই যখন ওদের আরাম করে পা ছড়াবার পক্ষে নিতান্ত অপরিসর ঠেকবে তখন ওরা কী করে বুঝবে আমার নগণ্য আঙিনাটুকুই আমার স্ত্রীর চোখে কত বৃহৎ বলে সে-বেচারি লজ্জায় ভয়ে ঘোমটা টেনে দেয়। আমাদের সেই রাত ভোর করে বেলা দশটা অবধি যাত্রা দেখা, দুপুর বেলা ঘুম দিয়ে রাত ন-টায় ওঠা, একটি গ্রামে একটা জীবন সাঙ্গ করেও তৃপ্তি না মানা, ভান্ডের মধ্যে ব্রহ্মান্ডকে দেখা—এসব ওদের কাছে তুচ্ছ মনে হবে। ‘সেকেলে’ বলে ওরা আমাদের অবজ্ঞা করবে।
তা করুক, কিন্তু একথা আমরা কোনো মতেই স্বীকার করব না যে, কোনো একটা যুগ কোনো আরেকটা যুগের চেয়ে সুখের, কোনো এক যুগের মানুষ কোনো এক যুগের মানুষের চেয়ে সুখী। পৃথিবী দিন দিন বদলে যাচ্ছে, সমাজ দিন দিন বদলে যাচ্ছে, কিন্তু উন্নতি? প্রগতি? পারফেকশন? তা কোনোদিন ছিলও না, কোনোদিন হবারও নয়। অতীত-পূজকরা বলবেন, সত্য যুগ ছিল না তো কোন আদর্শের আমরা অনুসরণ করব? ভবিষ্যৎ পূজকরা বলবেন, সত্য যুগ হবে না তো কোন আদর্শের অভিমুখে আমরা যাব? আমরা কিন্তু বর্তমান-প্রেমিক, আমরা বলি এইটেই সত্য যুগ এইটেই কলি যুগ, এটা ভালোও বটে মন্দও বটে। লাখ বছর পরে যারা আসবে তাদের যুগ এর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হলেও এমনি ভালোয়-মন্দে মেশা দুঃখে-সুখে বিচিত্র প্রেমে হিংসায় জটিল থাকবেই। আমরা চলার আনন্দে চলি, কারুর অনুসরণেও না, কারুর অভিমুখেও না। গতিটাই আনন্দের; শম্বুকের গতি আর পক্ষীরাজের গতি বেগের দিক থেকে ভিন্ন, আনন্দের দিক থেকে একই।
কিন্তু এটা মিথ্যা নয় যে, ক্রমেই আমাদের চলার বেগ বাড়ছে, ধীরে চলার আনন্দ গিয়ে ছুটে চলার আনন্দ আসছে। মানুষ এখন ঘর ভেঙে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ল, উদ্ভিদের মতো একঠাঁই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলতে চাইল না, পাখির মতো ঠাঁই ঠাঁই উড়তে উড়তে চলল। কোনো স্থানের প্রতি তার স্থায়ী আসক্তি রইল না। আগে ছিল গ্রামের প্রতি পেট্রিয়টিজম, তারপরে দেশের প্রতি পেট্রিয়টিজম, তারপরে পৃথিবীর প্রতি। দেখতে দেখতে এক-একটা দেশের বৈশিষ্ট্য চলে যাচ্ছে, দেশের লোক বিদেশে যাচ্ছে, বিদেশের লোক দেশে আসছে, কে যে কোন দেশে জন্মাচ্ছে কোথায় বিয়ে করছে কোনখানে মরছে তার ঠিক নেই। এই ইংল্যাণ্ডের এক অতি অখ্যাত অতি বিজন পল্লিগ্রামে এক তামিল চাষা—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও ঘোর অশিক্ষিত—ইংরেজ মেয়ে বিয়ে করে ছেলেপিলে নিয়ে সংসার করছে। সামান্য পুঁজি নিয়ে সে ঘর ছেড়েছিল, এখন বেশ সংগতিসম্পন্ন হয়েছে। এর ছেলেপিলে হয়তো কানাডায় বাসা বাঁধবে কিংবা অস্ট্রেলিয়ায়। কোন দেশের প্রতি তাদের পেট্রিয়টিজম যাবে? বাপের মাতৃভূমি না নিজের মাতৃভূমি না নিজের ছেলের মাতৃভূমি—কার প্রতি?
কত চীনা-মালয়-কাফ্রির ইংরেজ ছেলে দেখছি, কত কত ইংরেজের ফরাসি জার্মান জাপানি ছেলে দেখছি, কত সাদা রঙের আয়া লালচে কালো রঙের ছেলেকে ঠেলাগাড়ি করে বেড়াতে নিয়ে যায়, কত আর্য ধাঁচের মুখে মোঙ্গলীয় ধাঁচের ভুরু শোভা পায়। জগৎ জুড়ে একটা সংকর জাতি গড়ে উঠেছে, সে-জাতির নাম মানবজাতি। এই নতুন মানবের জন্যে যে নতুন সমাজ খাড়া হচ্ছে সে-সমাজের নীতিসূত্রও নতুন। সে সব নীতিসূত্র এরোপ্লেনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে তৈরি, গোরুর গাড়ির সঙ্গে অত্যন্ত বেখাপ্পা।
দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরো নর-নারীর মিলননীতি। গোরুর গাড়ির যুগের নর-নারী অল্পবয়সে বিবাহ করত পিতামাতার নির্বন্ধে, পরস্পরকে ছাড়া অন্য অনাত্মীয় স্ত্রী-পুরুষকে চিনতনা, জানত না, দেখত না; দুজনেই একস্থানে থেকে জীবন শেষ করত এবং একজন করত গৃহের অন্দরের কাজ, অন্যজন করত গৃহের সদরের কাজ। এরোপ্লেনের যুগের নর-নারী বিবাহ করে বেশি বয়সে পঞ্চশরের নির্বন্ধে; পরস্পরকে ছাড়া অন্য অনাত্মীয় স্ত্রী-পুরুষকে শৈশবে দেখতে পায় স্কুলে; যৌবনে দেখতে পায় অফিসে; বিবাহের পূর্বে দেখতে পায় ক্লাবে নাচঘরে টেনিস কোর্টে কাফে-রেস্তরাঁয়; বিবাহের পর দেখতে পায় অফিসের সহকর্মিণী বা সহকর্মীরূপে, একলা পথের সহযাত্রিণী বা সহযাত্রীরূপে, একলা প্রবাসের বান্ধবী বা বান্ধবরূপে। তারপর স্বামী-স্ত্রী এক স্থানে থাকতে পায় না, দুজনের দুই স্থানে জীবিকা। দুজনেই বাইরের কাজ করে, হোটেলে বাস করে, রেস্তরাঁয় খায় এবং সুবিধা না হলে দেখা করতে পায় না। সন্তানরা মেটার্নিটি হোমে জন্মায়, বোর্ডিং স্কুলে বাড়ে এবং বড়ো হলে জীবিকার সন্ধানে দেশ-বিদেশে বেড়ায়।
এহেন যুগে প্রেম ও সতীত্বের নীতি বদলাতে বাধ্য। প্রেম বা সতীত্ব থাকবে না এমন নয়, থাকবে, কিন্তু তাদের সংজ্ঞা হবে অন্যরকম। একনিষ্ঠতা সুখকর ছিল যখন স্বামী-স্ত্রী থাকত একস্থানস্থ এবং যখন অনাত্মীয়-আত্মীয়াদের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ ছিল অল্পই। এখন স্বামী লণ্ডনের দোকানে কাজ করে তো স্ত্রী কাজ করে চিকাগোর দোকানে, এবং উভয়েরই দোকানে বা দোকানের বাইরে বান্ধব-বান্ধবীর সংখ্যা নেই। একদিন যে-প্রেম আটলান্টিকের এক জাহাজে যেতে যেতে হয়েছিল, চিরদিন সে-প্রেম নাও টিকতে পারে এবং সে-প্রেমের পথে প্রলোভনও তো অল্প নয়, সুতরাং ডিভোর্স এবং পুনর্বিবাহ এবং আবার ডিভোর্স। কিংবা বিবাহটা একজনের সঙ্গে পাকা, মিলনটা অন্যান্য জনের সঙ্গে কাঁচা। এটা অবশ্য গোরুর গাড়ির ধর্মনীতির সঙ্গে এরোপ্লেনের হৃদয়গীতির সন্ধি করার প্রয়াস, কেননা ডিভোর্স আইন এখন গোরুর গাড়ির অনুশাসন অনুসারে কড়া এবং রোম্যান ক্যাথলিক ধর্মে নিষিদ্ধ। ভবিষ্যতে সন্ধির দরকার হবে না, গোরুর গাড়ি হটবেই, ডিভোর্সটা বিবাহের মতো সোজা হবে এবং বিবাহটা স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে বদলাবে। কেবল মুশকিল এই যে, মানুষের হৃদয়টা অত সহজে বদলাবার নয়—এডোনিসকে হারিয়ে ভেনাস কেঁদে আকুল হবে, ইউরিডিসকে খুঁজতে অর্ফিউস পাতালপ্রবেশ করবে, সীতার শোকে রঘুপতি স্বর্ণসীতাকেই হৃদয় দেবেন।
এতদিন নারী-নরের সম্বন্ধগুলো ছিল পারিবারিক—মাতা ও পুত্র, ভগিনী ও ভ্রাতা, স্ত্রী ও স্বামী, কন্যা ও পিতা। এখন এক নতুন সম্বন্ধের সূত্রপাত হয়েছে—সখা ও সখি। বিয়ের আগে বুঝতে পারা যাচ্ছে না শতেক সখির মধ্যে কোনটি প্রিয়তমা, কোনটি স্ত্রী। বিয়ের পরেও পদে পদে সন্দেহ হচ্ছে, যাকে বিয়ে করেছি সে স্ত্রী না সখি এবং যাদের সঙ্গে সখ্য হচ্ছে তাদের মধ্যে কোনো একজন সখি না স্ত্রী। গুরুজনের নির্বন্ধে যখন বিয়ে করা যেত এবং অনাত্মীয়া নারীর সঙ্গে পরিচয় ঘটত না, তখন যাকে পাওয়া যেত সেই ছিল স্ত্রী। কিন্তু এখন নিজের বিবাহের দায়িত্ব নিজের হাতে, ঠিক করতে গিয়ে ভুল করে ফেলা অতি সহজ এবং ভুল থেকে উদ্ধার পাওয়া অতি শক্ত। এখন অনাত্মীয়দের সঙ্গে নানা সূত্রে পরিচয়। বিয়ের আগে তো বটেই, বিয়ের পরেও স্ত্রীর সঙ্গে যত না সাক্ষাৎ হয় সখিদের সঙ্গে ততোধিক। স্ত্রী যখন নিকটে থাকে তখন শোবার সময় ছাড়া অন্য সময় দেখা করবার ফুসরত কোনো পক্ষেরই নেই। যে যার নিজের কাজে যায় ও রেস্তরাঁয় একা একা খায়। আর স্ত্রী যখন দূরে থাকে তখন তো দেখা হবারই নয়।
এই দূরে থাকাথাকিটাই বেশিরভাগ স্থলে ঘটছে। কেননা বিয়ের আগে স্ত্রী যে-কাজে বিশেষজ্ঞ হয়েছে বিয়ের পরে সে-কাজটি ছেড়ে দিয়ে স্বামীর সঙ্গে এক কর্মস্থল থেকে আরেক কর্মস্থলে ঘুরতে থাকা তার পক্ষে মস্তবড়ো ত্যাগ, এবং সে-ত্যাগে সমাজেরও ক্ষতি। সুতরাং প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রীর স্বামী যদি সংবাদপত্রের ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি হয় তো স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয় তার বৎসরান্তে এক বার। কিংবা কৃষক স্বামীর স্ত্রী যদি ভ্রাম্যমাণ চিত্রকর হয় তো স্বামীর সঙ্গে সে একেবারে বেশিদিন থাকতে পারে না। অথচ অভিনেত্রীর সঙ্গে প্রতিদিন নূতন পুরুষের আলাপ-বন্ধুতা এবং সংবাদদাতার সঙ্গে প্রতিদিন নূতন নারীর সাক্ষাৎ পরিচয়। এরূপ স্থলে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক—কে স্ত্রী, কে সখি। যাকে বিবাহ করেছি সেনাও হতে পারে স্ত্রী, যাকে বিবাহের আগে দেখিনি সেই হতে পারে সখির অধিক। যারা হৃদয় সম্বন্ধে অনেস্ট তাদের পক্ষে এটা এক বিষম সমস্যা, যারা সমাজকে ভয় করে ফাঁকি দিতে চায় তাদের পক্ষে কিছু নয়। তারা হয় চুপ করে সয়ে যায়, কাঁদে; নয় যতক্ষণ-না ধরা পড়ে ততক্ষণ ডুবে ডুবে জল খায়।
বিশ বছর আগেও স্ত্রী-পুরুষের বন্ধুতা ছিল সমাজের চোখে সন্দেহাত্মক; বিশেষত বিবাহের পরেও স্বামীর বা স্ত্রীর অনভিমতে। এখন বিবাহের সময় স্বামী-স্ত্রীতে স্পষ্ট বোঝাপড়া হয়ে যাচ্ছে যে স্ত্রীর সখাদের নিয়ে স্বামী কিছু বলতে পারবে না, স্বামীর সখিদের নিয়ে স্ত্রী কিছু বলতে পারবে না; পরস্পরের ওপরে বিশ্বাস রাখতে হবে। পরপুরুষের বা পরস্ত্রীর সঙ্গে বন্ধুতা কোনো কোনো স্থলে সংকট ঘটালেও মোটের ওপর সমাজসম্মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজসম্মত না হলে চলতও না কারণ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এখন একটা ব্যবধান অনিবার্য হয়ে পড়েছে—দূরত্বজনিত ব্যবধান। স্ত্রী আর গৃহিণী নয়, হোটেলবাসীর গৃহিণীর প্রয়োজন হয় না। স্ত্রী আর সচিবও নয়, ভ্রাম্যমাণ সংবাদদাতা তার অভিনেত্রী স্ত্রীর কাছে কী মন্ত্রণা প্রত্যাশা করতে পারে? স্ত্রী নিজের কাজে ব্যস্ত, বরং একজন সাংবাদিকার কাছে মন্ত্রণা প্রত্যাশা করা স্বাভাবিক। তারপর স্ত্রী যদি-বা সখি হয় তবু দূরে থাকে বলে বন্ধুতার সব দাবি মেটাতে পারে না। ধরো একসঙ্গে টেনিস খেলতে পারে না, সিনেমায় যেতে পারে না, হোটেলে খেতে পারে না, মোটরে বেড়াতে পারে না, অবসরকালে গল্প করতে পারে না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই যে অনিবার্য ব্যবধানটি, এটিকে পূরণ করতে পারে অন্য নারী বা অন্য পুরুষ—সে বিবাহিত-অবিবাহিত যা-ই হোক-না কেন। সেইজন্যে এখন পুরুষে পুরুষে বা নারীতে নারীতে বন্ধুতার মতো স্ত্রী-পুরুষে বন্ধুতাও চলতি হয়ে গেছে, এ নিয়ে কেউ কাউকে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য হয় না।
তাহলে দেখা যাচ্ছে সেকালের প্রেম ও সতীত্বের সংজ্ঞা একালে অচল। প্রথমত, প্রেম যে চিরস্থায়ী, এমনকী দীর্ঘস্থায়ী হবেই এমন কোনো কথা নেই। বিবাহের সময় এখনকার তরুণ-তরুণীরা তাদের ঠাকুরদাদা ঠাকুরমার মতো গম্ভীরভাবে প্রতিজ্ঞা করে না যে, যাবজ্জীবন পরস্পরের প্রতি একনিষ্ঠ থাকবেই। প্রতিজ্ঞা যদিও বাঁধানিয়ম মেনে করে, তবু লঘুভাবেই করে, মুখে যা বলে মনে তা বলে না। মনে মনে যোগ করে দেয়—‘আশা করি’। যেক্ষেত্রে ডিভোর্স যত সুলভ, সেক্ষেত্রে লঘুভাবটা তত বেশি। এই লঘুভাবটা না থাকলে মানুষ ভয়ে আধমরা হত। কেননা, এখন তো বিবাহ পিতা-মাতার নির্বন্ধে নয় যে ভুলের দায়িত্ব অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে ভগবানকে ডেকে আশ্বস্ত হবে। নির্বন্ধ যখন নিজেরই হাতে তখন ভুলের দায়িত্বও নিজেরই। একদিনের ভুলের জন্যে চিরজীবন প্রায়শ্চিত্ত করা অসহ্য। তা ছাড়া ভুল না-ই হোক, ঠিকই হোক, একদিনের ঠিক কি চিরদিন ঠিক থাকে? বিশ বছর বয়সের ঠিক কি ত্রিশ বছর বয়সেও ঠিক থাকে? দু-পক্ষই বদলায়, দু-পক্ষই নতুন সত্যকে পায়, পুরানো সত্যকে ভোলে। রল্যাঁর ‘আনেত’ যাকে প্রাণ ভরে ভালোবাসত তাকে কথা দিতে পারলে না যে চিরদিন তেমনি ভালোবাসবে, সেইজন্যে তাকে বিবাহই করতে পারলে না, অথচ তার ভালোবাসার চিহ্ন ধারণ করলে তার সন্তানের মা হয়ে।
দ্বিতীয়ত, সতী নারীর স্বামী ছাড়া অপর পুরুষের সঙ্গে তেমনি অন্তরঙ্গতা থাকতে পারে, যেমন অন্তরঙ্গতা এযাবৎ কেবল সখির সঙ্গেই সম্ভব ছিল। পরপুরুষকেও ভালোবাসা যায়, তার সঙ্গে গা-ঘেঁষে বসা যায়, তার কোলে মাথা রাখা যায়, অভিনয়কালে তাকে চুম্বন আলিঙ্গনও করা যায়, এমনকী অন্য সময়ও। স্বামীর সঙ্গে যেমন ব্যবহার সখার সঙ্গে তেমনি। অথচ সতী ধর্মের ব্যত্যয় হয় না। স্বামীর প্রতি প্রগাঢ়তম ভালোবাসা থাকে। এককথায় সখ্য প্রেম ও মধুর প্রেম পরস্পরবিরোধী নয়, একই হৃদয়ে দুয়েরই স্থান হতে পারে এবং এমনও একদিন হতে পারে যে সখ্য প্রেমই মধুর প্রেমে পরিণত হয়েছে, মধুর প্রেম সখ্য প্রেমে পর্যবসিত। সেরূপ স্থলে সম্বন্ধ পরিবর্তন অবশ্যপ্রয়োজন। স্বামী-স্ত্রী ঠাঁই ঠাঁই থাকার ফলে এমন ঘটা বিচিত্র নয়। স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই স্বতন্ত্র, দুজনেই স্বাবলম্বী, দুজনেই ভ্রাম্যমাণ। একদিন যে দুটি নক্ষত্র ঘুরতে ঘুরতে একস্থানে মিলেছিল চিরদিন তারা সেই স্থানে থাকতে পারে না, পরস্পরের থেকে সমান দূরত্ব রাখতে পারে না, দূরত্বের কম-বেশি ঘটে, অন্য নক্ষত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, এক সম্বন্ধ আরেক হয়ে ওঠে। যেক্ষেত্রে তেমন ঘটে না—দাম্পত্য ও সখ্য যেমন ছিল তেমনি থাকে, সেক্ষেত্রেও যে সতীত্বের পুরোনো আদর্শ খাটে না এটা স্বতঃসিদ্ধ। কেননা পুরোনো সতীত্বের সঙ্গে ছিল নিজের দ্বারা স্ত্রীকে স্বামীকে সাতপাকে ঘিরে রাখা, এখন অনেকখানি ঢিলে দিতে হচ্ছে, কোনো পক্ষেই বিশ্বস্ততার জন্যে পীড়াপীড়ি নেই, বিশ্বস্ততার জন্যে বাধ্যবাধকতা নেই, ওথেলো ক্রমশ সেকেলে হয়ে পড়ছে। স্বামী স্ত্রীর কাছে যা পাচ্ছে না অন্যের কাছে তা পাচ্ছে, স্ত্রী স্বামীর কাছে যা পাচ্ছে না অন্যের কাছে তা পাচ্ছে। চিরকুমার থাকলে সে কালে উপবাসী থেকে যেতে হত, চিরকুমার থাকলে একালে আধপেটা থাকতে পারা যায়—সখি থাকে কাছে। বিবাহ করলে সে কালে পেট ভরে উঠত, বিবাহ করেও একালে আধপেটা থাকতে হয়—স্ত্রী থাকে দূরে। একালের কুমারীদের অনেক দুঃখ থেকে অব্যাহতি মিলেছে, সেইজন্যে তারা বিবাহের জন্যে কেঁদে মরছে না এবং একালের বিবাহিতারাও অনেক সুখ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সেইজন্যে তারা সৌভাগ্যগর্বে বাড়াবাড়ি করছে না।
তবে ইংল্যাণ্ড ফ্রান্স প্রমুখ দেশে স্ত্রী-পুরুষের সাতিশয় সংখ্যা বৈষম্যের দরুন প্রেম-পরিণয়ের ক্ষেত্রে কতকটা কৃত্রিমতার উৎপত্তি হয়েছে বটে। কর্তারা দুনিয়া দখল করতে ব্যস্ত, যুদ্ধ না করলে তাদের চলে না, দেশের নারীসংখ্যার অনুপাতে পুরুষসংখ্যা যে কমতেই লেগেছে আর সেজন্যে নারী ও পুরুষ উভয়েরই যে নীতিভ্রংশ (demoralisation) হচ্ছে একথা কর্তারা বুঝেও বুঝছেন না। ছেলেরা জানে মেয়েরা তাদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি, সুতরাং বিবাহের গরজটা মেয়েদেরই বেশি, সাধতে হয় তো ওরাই সাধবে, তপস্যাটা একেবারে ও-তরফা। মেয়েরা জানে সকলের বরাতে বিবাহ নেই, বিবাহ যদি-বা হয় তবু স্বামীকে ধরে রাখতে পারা যাবে না, একজনকে হারালে আরেক জনকে পাবার আশা নেই, তপস্যাটা অনর্থক এ-তরফা। এর পরিণাম এই হচ্ছে যে, তপস্যাটাকে কোনো তরফই স্বীকার করছে না, হাতে হাতে যখন যা পাচ্ছে তখন তা নিচ্ছে। পরমুহূর্তে ছেলেরা ফেলে যাচ্ছে, মেয়েরা কান্না চাপছে। এ বড়ো নিষ্ঠুর খেলা। দু-পক্ষে সমান নিয়ম খাটছে না, একপক্ষ ফাউল করতে করতে অতি সহজে জিতছে, অপরপক্ষ ফাউল সইতে সইতে অতি সহজে হারছে। দু-পক্ষেরই নীতিভ্রংশ, তবু মেয়েরা দোষ ধরছে ছেলেদের, ছেলেরা দোষ ধরছে মেয়েদের। মেয়েরা বলছে, বাপ রে! একেলে ছেলেগুলোর কী দেমাক! এরা আমাদের খাওয়াবে না পরাবে না প্রতিপালন করবে না, শুধু আমাদের বিয়ে করে মাথা কিনবে, এরই জন্যে এত খোশামোদ! আমাদের ঠাকুরমাদের জন্যে আমাদের ঠাকুরদারা কী না-করতেন, ডুয়েল লড়ে প্রাণ বিপন্ন করতেন, যাকে অত কষ্টে পেতেন তাকে কত যত্নে রাখতেন! আর আমাদের এরা…! ছেলেরা বলছে, তোমরা সব স্বাধীনা স্বতন্ত্রা আলোকপ্রাপ্তা শি-ম্যান, আমাদেরকে না হলে তোমাদের যে চলে না এ তো বড়ো লজ্জার কথা! আর আমরা তো বেশ লক্ষ্মীছেলেই ছিলুম, তোমরা এতগুলোতে মিলে আমাদের মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছ, অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকা রোহিণীর কাকে ছেড়ে কাকে ধরা দেব আমরা পুরুষ চন্দ্রমারা!
৯
এদেশে এসে অবধি দেখছি বিপুলভাবে ধর্মচর্চা চলেছে। পাড়ায় পাড়ায় গির্জা, পথে-ঘাটে ধর্মপ্রচার, কুলির পিঠে ধর্মবিজ্ঞাপন। যে-জাতীয় সংবাদপত্রে কুকুর-দৌড়ের, শেয়ার মার্কেটের ও ডিভোর্স কোর্টের খবর থাকে সে-জাতীয় সংবাদপত্রেও ধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর। রেলে ও বাসে, অফিস থেকে ফেরবার সময় এক হাতে সান্ধ্য কাগজ ও অন্য হাতে ছয় পেনি দামের ধর্মগ্রন্থ নিয়ে একবার এটাতে ও একবার ওটাতে চোখ বুলিয়ে যেতে কত লোককেই দেখি। শুনতে পাই এখন ধর্মগ্রন্থগুলোর যত কাটতি, নভেল নাটকেরও নাকি তার বেশি নয়। বছর পনেরো-কুড়ি আগে নাকি এতটা ছিল না। যুদ্ধের পর থেকে হঠাৎ ধর্মচর্চার মরা গাঙে বান ডেকেছে। তা বলে অর্থচর্চা বা কামচর্চা কিছুমাত্র কমেছে এমন নয়। একসঙ্গে ত্রিমূর্তির উপাসনা চলেছে—গড, ম্যামন, Eros। ব্যাঙ্কে, এক্সচেঞ্জে, ডারবিতে, থিয়েটারে, নাচঘরে, হোটেলে, পার্কে, গির্জায় সর্বত্র লোকারণ্য, কোনো একটার ওপরে বিশেষ পক্ষপাত কারুর নেই; স্কুলে কলেজে লাইব্রেরিতে কারখানায় যেখানে যাই সেখানে লোকের ভিড়। মিউজিয়ামে চিত্রশালায় হাসপাতালে, অন্ধ-আতুর-অনাথাশ্রমে, যুদ্ধনিবারণী সভায় কোথাও কারুর আগ্রহ কম নয়। একটা জীবন্ত জাতির হাজারো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবই সমান জীবন্ত; যেমন তাদের বৈচিত্র্য তেমনি তাদের বৈপরীত্য—ভালো-মন্দ, সুন্দর-কুৎসিত, পদ্ম-পাঁক, ঐশ্বর্য-দৈন্য, প্রেম-হিংসা সবই একাধারে বিধৃত এবং সবই সমান প্রচুর; সেইজন্যে ধর্ম সম্বন্ধে সকলেই ভাবতে শুরু করেছে, একুশ বছর বয়সের ফ্ল্যাপার পর্যন্ত। শনিবারের দিন সন্ধ্যা বেলা যেসব যুবক-যুবতী পরস্পরের কোলে মাথা রেখে মাঠে বাগানে সকলের সামনে প্রেমালাপ করে, রবিবারের দিন সকাল বেলা সেইসব যুবক-যুবতী গির্জায় ভিড় করে অখন্ড মনোযোগের সহিত ধর্মোপদেশ শোনে, কলের পুতুলের মতো হাঁটু গাড়ে এবং সোমবারের দিনদুপুরে যখন তারা অফিসে গিয়ে পাশাপাশি কাজ করে তখন কেউ কারুর সঙ্গে ইঙ্গিতেও কথা বলে না, এমনই কঠোর ডিসিপ্লিন। কাল যদি যুদ্ধ বাঁধে ছেলেরা হাসিমুখে বন্দুক কাঁধে নিয়ে মরণযাত্রা করবে, মেয়েরা দেশের ভার কাঁধে নিয়ে ঘর ও বাহির দুই আগলাবে। সুখের সময় সুখ, দুঃখের সময় আশা, সবসময় প্রস্তুত ভাব—এই হচ্ছে ইংল্যাণ্ডের ধর্ম, ইউরোপের ধর্ম।
সামরিক সংস্কার বহুদিন হতে আমাদের সমাজে নেই, যখন ছিল তখন সমস্ত সমাজটার একটি বিশেষ অংশেই নিবদ্ধ ছিল। ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে ক্ষাত্রধর্মেরও উচ্ছেদ হয়েছে। ইউরোপের সমাজের সর্বশ্রেণির আবালবৃদ্ধবনিতা কিন্তু যুদ্ধে বিশ্বাসী, এ বিশ্বাসের ওপরে এদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা খাটে না, এ বিশ্বাস এদের প্রকৃতিগত; যুদ্ধহীন জগৎ এরা মনেও আনতে পারবে না। মানুষে মানুষে যুদ্ধ যে মন্দ তা এদের অনেকে বুদ্ধি দিয়ে বুঝেছে কিন্তু সংস্কার থেকে পায়নি। পশুতে-মানুষে যুদ্ধ যে মন্দ তা আমরা আড়াই হাজার বছর আগে বুদ্ধের সময় থেকে জেনেছি, এরা এখনও জানেনি। প্রকৃতিতে-পুরুষে যুদ্ধ যে মন্দ তা আমরা দৈববাদীরা কবে শিখলুম জানিনে, এরা কোনোদিন শিখবে না। এদের ভাবজগতেও আইডিয়াতে আইডিয়াতে যুদ্ধ। এদের ধর্ম যুদ্ধের জন্যে সদা প্রস্তুত থাকার ধর্ম। ন কিঞ্চিদপি বলহীনেন লভ্যম। নিশ্চেষ্ট যদি এক মুহূর্তের জন্যেও হও তবে অপরে তোমাকে মাড়িয়ে দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়ে যাবে।
ধর্ম ও রিলিজিয়ন এক জিনিস নয়। আমাদের ধর্মের নাম সনাতন ধর্ম, লোকমুখে হিন্দু ধর্ম; হিন্দু মানে ভারতীয়, সুতরাং ভারতীয় ধর্ম। আমাদের রিলিজিয়নগুলোর নাম বৈষ্ণব মত, শাক্ত মত, শৈব মত, সৌর মত, গাণপত্য মত ইত্যাদি। আমরা যদি খ্রিস্টীয় মত বা মহম্মদীয় মত নিই তবু আমরা হিন্দুই থাকব—ধর্মত হিন্দু; কিন্তু ধর্মের সঙ্গে ধর্মমতের তেমন সহজ সম্বন্ধ থাকবে না, কতকটা স্বতঃবিরোধ এসে পড়বে। আমাদের মধ্যে যাঁরা মুসলমান বা খ্রিস্টান হয়েছেন তাঁরা হিন্দুই আছেন, কিন্তু ভিতর থেকে সৃষ্টির স্ফূর্তি পাচ্ছেন না। ইচ্ছানুসারে ইসলামকে বা খ্রিস্টীয়নিয়ানিকে পরিবর্তন করতে পারছেন না, পরমুখাপেক্ষী হচ্ছেন। ইউরোপেরও এই দশা। ইউরোপের ধর্ম ও ধর্মমত অঙ্গাঙ্গি নয়, বিরুদ্ধ।
ইউরোপের প্রকৃতি হোমারের আমলে যা ছিল এখনও তাই, কিন্তু মাঝখানে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে প্যালেস্টাইন অঞ্চলের একটি বিশ্বাস। সে-বিশ্বাস ইউরোপের প্রকৃতির পক্ষে আড়ষ্টতাজনক। খ্রিস্টিয়ানিটির দ্বারা ইউরোপের অশেষ উপকার হয়েছে, কিন্তু খ্রিস্টিয়ানিটির পেষণে ইউরোপের আত্মা সৃষ্টির স্বতঃস্ফূর্তি পায়নি। ইউরোপের ধাত বিশ্লেষণশীল, এশিয়ার ধাত সংশ্লেষণশীল। ইউরোপের কীর্তি বিজ্ঞানে, এশিয়ার কীর্তি যোগে। ইউরোপ বিনা পরীক্ষায় কিছু মানে না, পরীক্ষার পর যা মানে তার বাইরে সত্য খুঁজে পায় না। আমরা অম্লানবদনে সব মেনে নিই, অধিকারী ভেদে মিথ্যাকেও বলি সত্য। ইউরোপ বিশ্বাস করে যোগ্যতমের ঊর্ধ্বতনে, আমরা বিশ্বাস করি সমন্বয়ে। এহেন যে ইউরোপ, তাকে তার নিজস্ব রিলিজিয়ন অভিব্যক্ত করতে না দিয়ে রাহুগ্রস্ত করে রাখল খ্রিস্টিয়ানিটি। সেই দুঃখে গোটা মধ্যযুগটা ইউরোপ অন্ধকারেই কাটাল। যেদিন গ্রিসকে দৈবাৎ পুনরাবিষ্কার করে সে আপনাকে চিনল সেদিন ঘটল Renascence, তারপর থেকে শুরু হল Reformation অর্থাৎ খ্রিস্টিয়ানিটির অগ্নিপরীক্ষা। সে-অগ্নিপরীক্ষা এখনও শেষ হয়নি, কিন্তু ধর্মচর্চার এই প্রাবল্য দেখে মনে হয় ও বোধ হয় নির্বাণ দীপের শেষ দীপ্তি, এরপরে হয় খ্রিস্টিয়ানিটিকে ভেঙে বিজ্ঞানের আলোয় নিজস্ব করে গড়া হবে, নয় বিজ্ঞানের ভিতর থেকে নতুন একটা রিলিজিয়ন বার করা হবে। বিজ্ঞান কথাটা আমি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছি। ইউরোপীয় দর্শনটাও বিজ্ঞানেরই তাঁবেদার, এবং বিজ্ঞান বলতে কেবল Physics ও Biology নয়, Psychology-ও বোঝায়। এখনও বিজ্ঞানের সামনে বিরাট একটা অজানা রাজ্য রয়েছে—মানুষের মন। ক্রমে ক্রমে যতই তাকে চেনা যাবে ততই একটা নতুন রিলিজিয়নের মালমশলা পাওয়া যাবে।
রিলিজিয়নের জন্যে মানবহৃদয়ের যে সহজ তৃষা তাকে শান্ত করবার ভার অপরকে দিলে চলে না; নিজেরই ওপরে নিতে হয় সে-ভার। ইউরোপের ভার এতদিন অন্যে বয়েছে। অন্যের ফরমাশ খেটে ও বাঁধা বরাদ্দ পেয়ে ইউরোপের তৃষা তো মেটেনি, অধিকন্তু খ্রিস্টিয়ানিটির ওপরে রাগ করে রিলিজিয়নের প্রতি জন্মেছে অনাস্থা—যেন রিলিজিয়নকে না হলেও মানুষের চলে। গত দেড়শো বছরের মধ্যে বিজ্ঞানের যে আশ্চর্য উন্নতি ঘটেছে সে-উন্নতি বহু দিনের রুদ্ধ জলের নিষ্কাশন, তাই সে এমন তাক লাগিয়ে দিয়েছে। গ্রিসের যদি মরণ না হত, তবে গ্রিসের ছেলেটি আয়ার কোলে অমানুষ না হয়ে তার নিজের কোলে দিন দিন শশীকলার মতো বাড়তে বাড়তে এতদিনে কেমন হয়ে উঠত জানিনে, কিন্তু খ্রিস্টিয়ানিটির ওপরে আধুনিক ইউরোপের মহা মনীষীদের এমন অশ্রদ্ধা ও রিলিজিয়নের ওপরে তাঁদের এমন অনাস্থা দেখতুম না। তাঁরা বলছেন, এই হতভাগা ধর্মমতটার জন্যেই এত যুদ্ধ, এত অশান্তি, এত গোঁড়ামি, এত কুসংস্কার। অন্ধবিশ্বাসী যাজকরা সেক্সকে পাপ বলে নিজেরা বৈরাগী হয়েছেন অথচ অন্যদের বলেছেন বহু সন্তানবান হতে, আর জনবৃদ্ধির ফলে যখন যুদ্ধ বেঁধেছে তখন এঁরাই দিয়েছেন মরণ-মারণের উত্তেজনা; এঁরা প্রচার করেছেন আত্মসম্মাননাশী উৎকট পাপবাদ—’We are born in sin,’ আমরা অধম, একমাত্র যিশুই ভরসা। গণতন্ত্রের এঁরাই শত্রু, স্বাধীন মানুষকে এঁরা সহ্য করতে পারেন না; দাস ব্যবসায়ের সমর্থক এঁরা; এঁরা বড়োলোকের মোসাহেব, ক্যাপিটালিস্টের বাহন ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। ফলে রাশিয়া থেকে চার্চ উঠে গেল, ফ্রান্সে চার্চের ওপরে কড়া নজর, ইংল্যাণ্ডে চার্চের প্রতিপত্তি যতটা দেখা যাচ্ছে কিছুদিন আগে ততটা ছিল না। তবে ইংল্যাণ্ডের চার্চ ইংল্যাণ্ডের স্টেটেরই মতো জনসাধারণের ইচ্ছাধীন। সেইজন্যে জনসাধারণকে খুশি রাখার জন্য এর অবিশ্রাম চেষ্টা।
চার্চ ও স্টেট এদেশের সমাজের এপিঠ-ওপিঠ। যাঁরা চার্চের নেতা তাঁরা পার্লামেন্টে বসেন, যাঁরা স্টেটের কর্ণধার তাঁরাও পার্লামেন্টে বসেন, পার্লামেন্টই হচ্ছে এদেশের সমাজপতিদের আড্ডা। আমাদের দেশে স্টেট ও সমাজ এক নয় এবং চার্চ আমাদের নেই। চার্চ যে এদের কতখানি তা আমরা দূর থেকে ঠিক বুঝতে পারব না, কেননা চার্চ মানে শুধু গির্জা নয়, চার্চ মানে সংঘ এবং সংঘ আমাদের দেশে বৌদ্ধ যুগের পর থেকে নেই। কেশবচন্দ্র সেন সংঘের পুনঃপ্রবর্তন করেন, আমাদের আধুনিক সংঘের নাম ব্রাহ্মসমাজ। ব্রাহ্মসমাজকে কেউ কেউ ব্রাহ্ম চার্চ বলে থাকেন, প্রবর্তক সংঘকেও চার্চ নাম দেওয়া চলে। কিন্তু হিন্দুসমাজকে হিন্দু চার্চ বলা চলে না। হিন্দুসমাজ কোনো একটা বিশেষ ধর্মমতকে প্রতিপদে মেনে চলবার জন্যে গঠিত একটা কৃত্রিম সংঘ নয়, হিন্দুর কাছে ধর্মমত একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার; স্বামী শাক্ত, স্ত্রী বৈষ্ণব ও সন্তান নাস্তিক হলেও হিন্দুসমাজ আপত্তি করে না। আজ যদি হিন্দুসমাজ সেকালের মতো জীবন্ত থাকত তবে স্বামী শৈব ও স্ত্রী মুসলমান হলেও আপত্তি করত না। হিন্দু ধর্ম ছিল দেশের ধর্ম, দেশে যে-কেউ বাস করত সে ছিল হিন্দু। জাতিভেদের উৎপত্তি হয়েছিল পেশাভেদের দ্বারা, পেশা বদলালে জাতিও বদলাত। কিন্তু ভারতবর্ষের কোনো অধিবাসীকেই অহিন্দু বলা হত না, যা-ই হোক-না কেন তার ধর্মমত বা রিলিজিয়ন।
হিন্দুসমাজ কোনো দিন ধর্মমত নিয়ে মাথা ঘামায়নি, কিন্তু দেশের আচারকে বা দেশের প্রথাকে শাক্ত বৈষ্ণব নির্বিশেষে মেনেছে। এখনও কি নিরাকারবাদী ব্রাহ্ম-আর্য-খ্রিস্টান-মুসলমান ভারতীয়রা সাকারবাদী শাক্ত বৈষ্ণবদের মতো একান্নবর্তী পরিবার ও তার অনিবার্য পরিণাম বাল্যবিবাহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত? একান্নবর্তী পরিবারের সঙ্গে বাল্যবিবাহ উঠে যাচ্ছে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের ফলে। এর সঙ্গে ধর্মমতের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নেই, কিন্তু ধর্মমত নির্বিশেষে অখন্ড হিন্দুসমাজের ঐতিহাসিক সম্বন্ধ ছিল। একটু খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে খ্রিস্টান-মুসলমান-বৈষ্ণব-শাক্ত সকল ভারতীয়ের মধ্যে একই সংস্কার বিদ্যমান। তবু কয়েকটা ধর্মমতকে হিন্দু নাম দিয়ে অন্যগুলিকে অহিন্দু নাম দেওয়া হচ্ছে ধর্মমতকে ধর্ম বলে ভুল করে।
চার্চ বা সংঘ হচ্ছে একটা ধর্মমতের বা রিলিজিয়নের দ্বারা পরিচালিত সমাজ, জাতীয় প্রকৃতি বা জাতীয় ধর্মের সঙ্গে তার রক্ত-সম্পর্ক নেই। চার্চ অনায়াসেই আন্তর্জাতিক হতে পারে। রোমান চার্চ একদিন সমস্ত ইউরোপকে আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক উভয়ভাবেই শাসন করছিল। ক্রমশ আধিভৌতিক দিকটাকে নিয়ে আধুনিক ধরনের স্টেট গড়ে ওঠে, চার্চের কাজ লাঘব হয়। তারপর নানা দেশে স্টেটের সঙ্গে চার্চের নানা বিচ্ছেদ দেখা দেয়। কোথাও স্টেট চার্চকে গ্রাস করে, কোথাও স্টেট চার্চকে ভাতে মারে, কোথাও স্টেট চার্চকে কোনোমতে টিকে থাকবার অনুমতি দেয়। ইংল্যাণ্ডে কিন্তু স্টেট ও চার্চ বেশ বনিবনা করে চলছে, চার্চ অবশ্য এখন স্ত্রৈণ স্বামীর মতো স্টেটের বিশেষ অনুগত, নইলে রাশিয়ার চার্চের মতো তাকেও ভিটে ছাড়া হয়ে বনে পালাতে হত। কিন্তু অত্যাধুনিক স্ত্রীদের খোশমেজাজের ওপর অতটা ভরসা রাখা স্বামী মাত্রেরই পক্ষে ভয়াবহ। ইংল্যাণ্ডের চার্চও কবে disestablished হয়ে মনের দুঃখে বনে যাবে বলা যায় না, স্টেটের জুলুম দিন দিন বাড়ছে।
খ্রিস্টীয় আদর্শের যাঁরা সমর্থক তাঁদের অনেকে বলছেন, Christianity never had a trial, খ্রিস্টীয় আদর্শকে আমরা গ্রহণই করিনি এতদিন, আমরা গ্রহণ করেছি চার্চের কর্মকান্ড, আমরা শরণ করেছি সংঘকে। চার্চের দ্বারা খ্রিস্টের ব্যক্তিত্ব এতকাল ঢাকা পড়ে এসেছে, খ্রিস্টের সরল উক্তিগুলিকে চার্চের মহামহোপাধ্যায়রা টীকাভাষ্যের দ্বারা জটিল করে কুটিল করে ব্যাখ্যা করেছেন। ওল্ড টেস্টামেন্টের সৃষ্টিতত্ত্ব ও নিউ টেস্টামেন্টের ত্রাণতত্ত্বকে গোড়াতে স্বীকার না করেও খ্রিস্টের অনুজ্ঞা পালন করা সম্ভব, খ্রিস্টকে অনুসরণ করা সম্ভব। খ্রিস্টের জন্মঘটিত রহস্যগুলো সম্বন্ধে খ্রিস্ট স্বয়ং কিছু বলেননি, চার্চই যা-খুশি বানিয়েছে। নিজের প্রতিপত্তির জন্যে চার্চ খ্রিস্টকে এক্সপ্লয়েট করেছে, খ্রিস্টকে ইচ্ছামতো ভেঙে গড়েছে। আমরা সত্যিকার খ্রিস্টকেই চাই, আমরা চার্চের হস্তক্ষেপ সহ্য করব না। আমরা খ্রিস্টের সৃষ্ট খ্রিস্টিয়ানিটিকেই চাই। আমরা চার্চের বানানো খ্রিস্টিয়ানিটি বর্জন করব। চার্চের হাত থেকে রিলিজিয়নকে উদ্ধার করে তাকে ব্যক্তির ক্ষুধা-তৃষ্ণার বিষয় করবার দিকে অনেকেরই দৃষ্টি পড়েছে, কিন্তু এতকালের চার্চকে এককথায় বিদায় দেওয়া যায় না, তুলে দেওয়া যায় না। তা ছাড়া সংঘের মধ্যেও একটা সত্য আছে, সংঘবদ্ধ সাধনার একটা মূল্য আছে, ব্যক্তি ও সমাজের মাঝখানে হয়তো চিরকাল একটা মধ্যস্থ থেকে যাবেই, সেটার নাম গ্রুপ বা পার্টি বা সম্প্রদায় যা-ই হোক-না কেন। নির্জলা ব্যক্তিতন্ত্রবাদ বা নির্জলা সমাজতন্ত্রবাদ সফল হতে না জানি কত কাল লাগবে। হিন্দুসমাজের পেশাগত জাতি একদিন জন্মগত জাতি হয়ে না দাঁড়িয়ে থাকলে হিন্দুসমাজই জগৎকে একটা মস্ত সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকত।
রিলিজিয়নের ক্ষেত্রে পূর্ব দেশের কাছ থেকে কোনোরকম দিশা পাওয়া যায় কি না এই নিয়ে অনেক তত্ত্বপিপাসু ব্যক্তি গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন, বুদ্ধকেও নিয়ে নাড়াচাড়া করা হয়েছে। প্রায় দু-হাজার বছর রিলিজিয়ন বলতে কেবল খ্রিস্টিয়ানিটিই যাঁরা বুঝেছেন তাঁদেরও মুখ বদলাবার পক্ষে পৃথিবীর অপরাপর রিলিজিয়নগুলোর মূল্য থাকতে পারে, কিন্তু সত্যি সত্যিই যে তাঁরা স্থায়ীভাবে এগুলিকে গ্রহণ করবেন এমন ভাবা ভুল। কারণ ওসব রিলিজিয়ন খ্রিস্টিয়ানিটিরই মতো অন্য মাটির গাছ; ইউরোপের মাটিতে রোপণ করলে ওদের বৃদ্ধি তো হবেই না, ইউরোপের নিজের ফসল ফলাবার জন্যে যথেষ্ট জায়গাও থাকবে না। ইউরোপের ধর্মের সঙ্গে বাইরের ধর্মমতের নাড়ির বাঁধন নেই, তেলে-জলে মিশ খাবার নয়। ইউরোপের প্রকৃতি নিজের ফুল নিজে ফোটাতে পারে তো নিজেই একদিন ফোটাবে; অন্যের ফুল আদর করে দেখতে পারে, পরতে পারে, কিন্তু বাঁচিয়ে রাখতে, তাজা রাখতে পারবে না। ইউরোপের আপনার জিনিস তার ফিলজফি, তার বিজ্ঞান। পরের কাছে ধার-করা থিয়োলজিকে সে এখনও আপনার করতে পারলে না, দর্শন-বিজ্ঞানের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারল না। আবার যদি ধার করতে যায় তো দর্শন-বিজ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে ধার করবে, নিজের ধাতের ভিত্তির ওপরে পরের মতের সৌধপ্রতিষ্ঠা করবে; ভূমিকম্পে হয় তো ভিত্তি টলবে না, সৌধ ধসে পড়বে। ইউরোপের হাড়ে হাড়ে পুরুষকার, আমাদের হাড়ে হাড়ে দৈব। ইউরোপের হাড়ে হাড়ে দ্বন্দ্বভাব শত্রুভাবের সাধনায় সত্যের উপলব্ধি, আমাদের হাড়ে হাড়ে সন্ধিভাব মিত্রভাবের সাধনায় সত্যের উপলব্ধি। ইউরোপ অর্জন করে উড়িয়ে দেয়, আমরা অমনি ভিতর থেকে পাই, সঞ্চয় করি। আমাদের উপলব্ধি ইউরোপ যদি নেয় তো নিজের মনের মতো করে নেবে, খ্রিস্টিয়ানিটির আত্মাটুকু বাদ দিয়ে যেমন ধড়টাকে চার্চে ঝুলিয়ে রাখল এবং নিজের যুদ্ধপ্রিয়তাকে তার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে তাকে বেতাল করে তুলল, আমাদের বেদান্ত বা বৈষ্ণব তত্ত্ব সম্বন্ধেও তাই করবে, এবং নিজের বিজ্ঞানদর্শনের দ্বারা ডিস্টিল করে ধোঁয়া ছাড়া আর কিছুই তার গ্রহণ করবে না। সেইজন্যেই আমার মনে হয় ইউরোপকে আমরা মুরুব্বির মতো শিক্ষা দিতে পারব না, কেবল বন্ধুর মতো সাহায্য করতে পারব। আমাদের সাহায্যে ইউরোপ যদি নিজের রিলিজিয়ন নিজে সৃষ্টি করে, আর ইউরোপের সাহায্যে আমরা যদি আমাদের রিলিজিয়নগুলোকে বিজ্ঞান শোধিত করে নিই, তবে অতি দূর ভবিষ্যতে দুই মহাদেশের আত্মার মিলন হবে নিবিড়তম; দুটিতে হবে হরিহরাত্মা। তার পরে যখন আরও দূর ভবিষ্যতে দুই মহাদেশের প্রকৃতি এক হয়ে আসবে, ধর্ম এক হয়ে আসবে, তখন দুটিতে হবে এক দেহ-মন, একাত্ম।
এই মুহূর্তে রিলিজিয়ন সম্বন্ধে ছোটো-বড়ো ইতর-ভদ্র সকলেই কিছু কিছু ভাবছে; কিন্তু এখনও সে-ভাবনা তেমন ঐকান্তিক হয়নি, যেমন হলে নতুন একটা রিলিজিয়নের জন্মলক্ষণ দেখা যেত। মাত্র দেড়শো বৎসরের বিজ্ঞানচর্চা জীবনকে এখনও যথেষ্ট উদ্ভ্রান্ত করেনি, দেড়শো বছর আগের গোরু-ঘোড়ার গাড়ি থেকে মাত্র এরোপ্লেন অবধি উঠেছে, এখনও অসংখ্য উদ্ভাবন বাকি। আগামী দেড়শো বছরে হয়তো আকাশে বাড়ি তৈরি করে, বাগান তৈরি করে ফুল ফুটিয়ে দেবে। জীবন যতই জটিল হয় রিলিজিয়নকে ততই দরকার হয়—রিলিজিয়ন খুলে দেয় গ্রন্থি, রিলিজিয়ন করে তোলে সরল। সরলীকরণের আকাঙ্ক্ষা এখনও তীব্র হয়নি বটে, তবু সরলীকরণ যে দরকার সে জ্ঞান সকলেরই কতকটা হয়েছে। ভারতবর্ষে গান্ধীর জন্ম, তিনি যন্ত্রের প্রতাপ সামান্যই দেখেছেন। তাঁর বিশ্বাস যন্ত্রকে না হলেও মানুষের চলে। তিনি জীবন থেকে যন্ত্রকে ছেঁটে ফেললেই সরলীকরণের সাক্ষাৎ পান। কিন্তু ইউরোপে যেসব মনীষীর জন্ম তাঁরা যন্ত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিত, তাঁদের জন্মের বহু পূর্ব হতেই যন্ত্র ও জীবন এক হয়ে গেছে, যন্ত্রকে ছেঁটে ফেলা ও শরীরের চর্ম তুলে ফেলা তাঁদের পক্ষে একই কথা। সরলীকরণের জন্যে তাঁরা যন্ত্রকে ছেড়ে যন্ত্রীর দিকেই দৃষ্টি দিচ্ছেন, যন্ত্রকে রেখেও জীবনকে কতখানি সরল করা যায় এই হচ্ছে তাঁদের প্রশ্ন।
সেইজন্যে দেখা যায় ধনীদের ঘরেও আসবাবের বাহুল্য কমছে, সুন্দর দেখে অল্প কয়েকটি আসবাব রাখা হচ্ছে। মেয়েদের পোশাকের ওজন কমছে, বহর কমছে; সুরুচিকর দেখে অল্প কয়েকখানা কাপড় পরা হচ্ছে। খোলা আকাশ, খোলা হাওয়া, খোলা মাঠের টানে ছেলেরা পায়ে হেঁটে পৃথিবীময় ঘুরছে। অল্প কাপড়, সাদাসিধে খাবার, প্রচুর শারীরিক শ্রম, খোলা জায়গায় নিদ্রা—এইসব হল ইয়ুথ মুভমেন্টের মূলসূত্র। জার্মানি অঞ্চলে কাপড় জিনিসটাকে যথাসম্ভব বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলেছে; অথচ ওই ভয়ানক শীতে উলঙ্গ ব্যায়াম, উলঙ্গ সাঁতার, অর্ধোলঙ্গ নাচ ক্রমেই চলতি হচ্ছে। খাদ্যগুলো ক্রমেই কাঁচার দিকে যাচ্ছে। বাসগৃহগুলোর জানালাগুলো বড়ো হতে হতে এত বড়ো হয়ে উঠছে যে ঘরে থেকেও বাইরে থাকা যাচ্ছে। বৈঠকখানায় বরফ বিছিয়ে স্কেট করা হচ্ছে। দারুণ শীতেও বরফের মতো ঠাণ্ডা জলে স্নান করে উঠে অল্পসংখ্যক পাতলা কাপড় পরা হচ্ছে। এককথায় দেহটাকে লোহার মতো মজবুত করে গড়া হচ্ছে। গ্রিক মূর্তির মতো সবল সুষম সুন্দর দেহ এখনকার আদর্শ। নর-নারী উভয়েই এ আদর্শ গ্রহণ করছে। খ্রিস্টিয়ানিটি দেহকে তাচ্ছিল্য করে ইন্দ্রিয়কে রিপু বলে উপবাসকে শ্রেয় বলে আত্মনিগ্রহকে ধর্ম বলে চালিয়েছিল, কিন্তুএ ধর্ম ইউরোপের প্রকৃতিগত নয়। সেইজন্যে এর বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিক্রিয়া চলেছে। সেক্সকে খ্রিস্টিয়ানিটি এত ঘৃণা করেছিল বলেই সেক্সকে হঠাৎ এত শ্রদ্ধা করা হচ্ছে। প্রতিক্রিয়ার সময় কোন জিনিসের যে কত দাম তা স্থির করা শক্ত হয়। মানুষের মধ্যে যে-ভাগটা পশু সে-ভাগটাকে অযথা নিন্দা করে অযথা নির্যাতন করা হয়েছে; পরিণামে আজ সেই ভাগটাই সবচেয়ে বড়ো ভাগ, হয়তো সেইটেই সব এমন কথাও শুনতে হচ্ছে। গ্রিককে অক্ষুণ্ণ রেখে তার ওপরে খ্রিস্টানকে ঢেলে সাজালেই হয়তো সোনায় সোহাগা হয়, কিন্তু কোনো পক্ষের গোঁড়ারা সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমি ছাড়বেন না।
সরলীকরণ বলতে যারা পেগানিজম বুঝে দেহের বোঝা লাঘব করছে, তারাই রিলিজিয়নের মোহ এড়াতে না পেরে গির্জায় যাচ্ছে, ধর্মগ্রন্থ পড়ছে, ধর্মালোচনা করছে, ঘরে বসে রেডিয়োতে ধর্মকথা শুনছে। শ্যাম ও কুল দুই-ই রাখছে, কিন্তু দুয়ের সমন্বয় করতে পারছে না। দু-হাজার বছরের অভ্যাস বড়ো সহজ কথা নয়, বাঘকে আফিম অভ্যাস করালে বাঘও হাই তোলে। আফিমের বদলে কোকেন ধরিয়ে লাভ নেই, প্রাচ্য রিলিজিয়ন মাত্রেই ইউরোপের পক্ষে পরধর্ম। তার যখন ক্ষুধা প্রবল হবে সে তখন নেশার বদলে খাদ্য খুঁজে নিলেই সবদিক থেকে ভালো। সে-খাদ্য তার নিজের ভাঁড়ারঘরে মালমশলা আকারে পড়ে রয়েছে, নিজের রান্নাঘরে নিয়ে পাক করে নিলে পরে পরিপাকযোগ্য হবে। ইউরোপের রিলিজিয়ন ইউরোপের লাইব্রেরি-ল্যাবরেটরি-স্টুডিয়ো-স্টেডিয়াম থেকেই ভূমিষ্ঠ হবে, গির্জা-মসজিদ-মন্দির থেকে নয়।
১০
পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচন অবশ্য বছরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন হয় না, কিন্তু এক নির্বাচনের পর থেকে আরেক নির্বাচন অবধি প্রত্যেকটি দিন সমস্ত দেশটাই নির্বাচনের মালা জপতে থাকে। এ দৃশ্য সহজে চোখে পড়ে না কেননা চোখ কাড়বার মতো দৃশ্য এটি নয়, ইংল্যাণ্ডের মতো দেশে দুটি চোখ নিয়ে বাস করা এক ঝকমারি। সম্প্রতি এখানে বৈশাখ মাসের গরম, ষোলো-সতেরো ঘণ্টা সূর্যালোক, তাই মাস চার-পাঁচ আগে যে-সময় ঘুমুতে যেতুম, সেই সময় বেড়াতে বেরিয়ে দেখি রাত্রের আহার শেষ করে লোকে সূর্যের আলোয় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুনছে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে এক-একজন বক্তা এক-একখানা টুল বা চেয়ার বা ভাঙা বাক্স বা কোনোরকম একটা উঁচু আসন জোগাড় করে তার উপরে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন। দেখামাত্র আমাদের দেশের সঙ্গে দুটো তফাত ধরতে পারি। প্রথমত, বক্তা যে-দলেরই হন তিনি যুক্তি দেখান—দেখাতে বাধ্য হন। প্রশ্নের চোটে তাঁকে নাকাল করবার মতো শ্রোতার অভাব হয় না। নানা দলের লেখা বক্তৃতা পড়ে শুনে প্রত্যেকেরই চোখ-কান এতটা সজাগ হয়েছে যে, কারুর চোখে ধুলো দেওয়া বা কানে মন্তর দেওয়া সোজা নয়। ভাবপ্রবণতা এ জাতটার ধাতে নেই, গোলদিঘির বক্তাদের হাইড পার্কে দাঁড় করিয়ে দিলে শ্রোতা নয় দর্শক যদি-বা জোটে তবে তাদের এক জনেরও চোখের পাতা ভিজবে না, কন্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হবে না, শিরায় বিদ্যুৎ খেলবে না। সুতরাং বক্তারা শ্রোতাদের অন্যরকম দুর্বলতার সুযোগ নেন। ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণ হয় বোঝে যুক্তি-তথ্য, নয় বোঝে মদ। সেকালে মদ খাইয়ে ভোট আদায় করা হত, একালে ওসব উঠে গেছে, তাই যুক্তি-তথ্যকে এমন কৌশলে পরিবেশন করতে হয় যাতে শ্রোতার বা পাঠকের নেশা ধরবে। Statistics-এর মারপ্যাঁচে মিথ্যাকে সত্য ও সত্যকে মিথ্যা করতে না জানলে ইংল্যাণ্ডের ভবিকে ভোলানো যায় না। তাকে ভয় পাওয়ানোর চেষ্টা বৃথা, কান্না পাওয়ানোর চেষ্টা হাস্যকর। বক্তারা তর্জন-গর্জন বা বিলাপ প্রলাপের দিক দিয়েও যান না, তাঁরা নিপুণ ক্যানভাসারের মতো বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি ঘুলিয়ে দেন।
দ্বিতীয়ত, বক্তারা অত্যন্ত আন্তরিকতাসম্পন্ন নাছোড়বান্দা প্রকৃতির লোক। গালাগালি সহ্য করা তো তুচ্ছ কথা, কোনোমতেই তাঁরা মেজাজ হারাবেন না, বেফাঁস কথা বলে বসবেন না, তাঁদের ব্যক্তিগত মান-অপমানের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবেন না; তাঁদের একমাত্র ভাবনা তাঁদের দল কেমন করে পুরু হবে। অথচ তাঁরা ভাড়াটে বক্তা নন; হয়তো পেশাদার বক্তাও নন; কেউ দুপুর বেলা মাটি কেটে এসেছেন, কেউ গাড়োয়ানি করে এসেছেন, এখন চান দলের লোকের সাহায্য করতে। রাজনৈতিক দলাদলির ঠিক নীচে ধর্মনৈতিক দলাদলি। কিন্তু সব দলেই অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবক অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবিকা আছে—তারা দলের জন্যে আর কিছু ত্যাগ করুক না করুক অন্তত অসহিষ্ণুতাটুকু ত্যাগ করেছে। তাদের দলের তালিকায় যদি একটাও নাম বাড়ে তবে বোধ করি তারা জুতোর মারও সহ্য করবে। মিশনারিরা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে, এমন গ্রাম নেই যেখানে তারা ধর্মপ্রচার করেনি, এমন ভাষা নেই যে-ভাষার বর্ণমালা না থাকলেও সে-ভাষায় তারা বাইবেল ছাপায়নি। এই অসাধারণ উদ্যোগিতা এদের জাতিগত। ভোট দেওয়ার অধিকার লাভ করবার জন্যে এদের মেয়েরা পঞ্চাশ বছর ধরে কী অসীম ধৈর্যের সঙ্গে, কী অসীম নিষ্ঠার সঙ্গে দিনের পর দিন খেটে এসেছে। জন কয়েকের প্রচেষ্টা ক্রমশ লক্ষ লক্ষ জনের হল, তারপরে জয়। কিন্তু ওইটুকুতে তারা সন্তুষ্ট হয়নি, তারা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সব বিষয়ে সমান অধিকারী করবে, তার আগে থামবে না। এখন তাদের যুদ্ধ চলেছে স্ত্রী-পুরুষকে সমান খাটুনির বিনিময়ে সমান মজুরি দেওয়া নিয়ে; বিবাহিতা নারীকে বিবাহিত পুরুষের মতো চাকরি করতে দেওয়া নিয়ে; সবরকম জীবিকায় স্ত্রী-পুরুষকে সমান শর্তে স্থান দেওয়া নিয়ে। এদের শ্রমিকরাও এমনই নাছোড়বান্দা প্রকৃতির যোদ্ধা। নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্যে তারা সর্বক্ষণ সচেষ্ট। আমাদের শ্রমিকদের এখন যে-অবস্থা, এদের শ্রমিকদেরও এক শতাব্দী আগে সেই অবস্থা ছিল। কিন্তু তারা গ্রামে ফিরে গিয়ে সামান্য জমিজমাকে শত ভাগ করে মান্ধাতার আমলের চরকাখানাকে শত বার ঘুরিয়ে ফল পেলে না, কলকারখানার কাছে slum তৈরি করে ওইখানেই জেদ করে পড়ে রইল, এবং জেদের সঙ্গে লড়াই করতে লাগল। এখনও তাদের অবস্থার যেটুকু উন্নতি হয়েছে সেটুকু তাদের মনঃপূত নয়, তাই তাদের লড়াই থামছে না, তারা সব বিষয়ে ধনিকদের মতো না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালাবেই। ধনিকরাও চুপ করে বসে থাকেনি, এরা ডালে ডালে চলে তো ওরা পাতায় পাতায় চলে, সুতরাং লড়াই কোনো কালে থামবার নয়।
লড়াই যারা করে তারা প্রাণের দায়ে করে। তাই বক্তারা প্রাণপণে বক্তৃতা দেয়। সেটা তাদের শৌখিন বাচালতা নয়, সেজন্য তারা কারুর হাততালির আশা রাখে না। কেউ না শুনলেও তারা রণে ভঙ্গ দেয় না, যে-পর্যন্ত একটিও শ্রোতা থাকে সে-পর্যন্ত তাদের বক্তৃতা চলতে থাকে, বরং তখনই তাদের বক্তৃতা জোরালো হয়। আমাদের দেশে মাত্র দুটি শ্রেণির লোককে আমি এমন নাছোড়বান্দা হতে দেখেছি—পান্ডা আর ঘটক। অভিমান কাকে বলে কেবল এই দুই শ্রেণির লোক জানে না; বাকি সকলেই অল্পবিস্তর অভিমানী। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে পরের উপর মান করলে ঘরের উনুনে হাঁড়ি চড়ে না। তাই অভিমান কথাটা ইংরেজি ভাষায় নেই। এতে ইংরেজি ভাষার ক্ষতি হয়েছে কি না জানিনে, কিন্তু ইংরেজ জাতটার বৃদ্ধি হয়েছে। দুনিয়ার সর্বত্র জাহাজ না-পাঠালে ইংল্যাণ্ডকে প্রায়োপবেশনে মরতে হয়, সুতরাং ইংল্যাণ্ডকে দুনিয়ার সকলের দ্বারে ধাক্কা দিতেই হয়—’Knock and it shall be opened unto you.’ এমনি করে ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকার বন্ধ দুয়ার খুললে, ভারতবর্ষকেও ঘুমাতে দিলে না।
যে-কারণে ইংল্যাণ্ডকে বাইরে ধাক্কা দিয়ে ফিরতে হয় সেই কারণে ইংল্যাণ্ডের লোককে ঘরের ভান্ডারে ভাগ বসাবার চেষ্টা করতে হয়। পার্লামেন্টের হাতে ভান্ডারের চাবি। চাবিটার জন্যে দিনরাত লড়াই। এক মুহূর্ত ঢিলে দিলে সর্বনাশ। চাবিটা যাদের হাতে আছে তাদের যেমন ভাবনা, চাবিটা যাদের হাতে নেই তাদেরও তেমনি ভাবনা। আমাদের দেশে রাজনীতিকে লোকে জীবন-মরণের ব্যাপার বলে ভাবতে শেখেনি। আমাদের কাজের লোকেদের শেষজীবন কাটে কাশীতে, বৃন্দাবনে। রাজনীতি চর্চাটা এখনও আমাদের চোখে দেশের প্রতি একটা অনুগ্রহ; সে-অনুগ্রহটুকু যাঁরা করেন তাঁরা একলম্ফে দেশপূজ্য। এদেশে কিন্তু ওটা ধর্মচর্চার মতো অবশ্যকরণীয় ব্যাপার; যাঁরা করেন তাঁরা নিজের বা নিজের দলের বা নিজের দেশের গরজে করেন; সেজন্যে বাহবা পাওয়ার কথাই ওঠে না; দেশপূজ্য হওয়া দূরে থাক দেশের কাজে লাঞ্ছনা পাওয়াটাই ঘটে। লয়েড জর্জ কাশী-বৃন্দাবনে না গিয়ে পার্লামেন্টে যান, সেজন্য তাঁকে ছেড়ে কথা কইতে হবে কেন? তাঁর পুণ্যার্জনের লোভ আছে তাই তিনি ভারতবর্ষ হলে কাশী যেতেন, ইংল্যাণ্ড বলে পার্লামেন্টে গেলেন। লোকে যেমন কাশীবাসীকে ছেড়ে কথা কয় না, পার্লামেন্টবাসীকেও ছেড়ে কথা কয় না। বলডুইন দেশের জন্যে ত্যাগ বড়ো কম করেননি, ইংল্যাণ্ডের আদর্শে সে-ত্যাগ চিত্তরঞ্জনের ত্যাগের চেয়ে ছোটো নয়। তবু তাঁকে তাচ্ছিল্য করতে রাস্তার টম ডিকও পশ্চাৎপদ নয়। লয়েড জর্জ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দুর্দিনে তাকে রক্ষা করলেন অথচ তাঁকে ঠাট্টা করা ও খ্যাপানো এখানকার একটা ফ্যাশন।
ইংল্যাণ্ড দিন-কে-দিন যতই গণতান্ত্রিক হচ্ছে ততই তার মহাপুরুষভীতি বাড়ছে। মাঝারি মানুষ ছাড়া অন্য কোনো মানুষ ক্রমশই ইংল্যাণ্ডের মাটিতে অসম্ভব হয়ে আসছে। একজন ক্রমওয়েলকে বা একজন মুসোলিনিকে ইংল্যাণ্ড দু-চক্ষে দেখতে পারবে না; এমনকী একজন পিলকে বা গ্ল্যাডস্টোনকেও না। ইংল্যাণ্ডের মতো অতি স্বাধীন দেশে কোনো মানুষই যথেষ্ট স্বাধীন নয়। হাজারো আইনকানুন ও সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের দশজনের একটা mass suggestion-ও আছে, সমাজের দশজন চায় না যে তাদের মধ্যে কোনো একজন সর্বেসর্বা হোক কিংবা বাকি ন-জনের চেয়ে মাথায় উঁচু হোক। গণতন্ত্রের আন্তরিক ইচ্ছা—কেউ বামন হবে না, কেউ দৈত্য হবে না, সবাই প্রমাণ সাইজ হবে। তাই ইংল্যাণ্ডের মহাপুরুষরা কেবল রাজনীতিতে নয়, কোনো বিষয়েই আকাশস্পর্শী হচ্ছেন না। সাহিত্যক্ষেত্রে গত শতাব্দীর ব্রাউনিং, টেনিসন, কার্লাইল, ডিকেনসের দোসর দেখা যাচ্ছে না, বিজ্ঞানেও কোনো একজন লোক ডারুইনের মতো অতি অসাধারণ নন। অথচ মাঝারি সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক ও রাজনীতিজ্ঞেরা গত শতাব্দীর চেয়ে এ শতাব্দীতে সংখ্যায় অধিক ও উৎকর্ষে বড়ো। তাঁরা লোকের নিন্দা প্রশংসা পাচ্ছেন, কিন্তু বিশেষ শ্রদ্ধা বা বিশেষ অশ্রদ্ধা পাওয়ার মতো মহান তাঁরা নন। তাঁদের নিয়ে এক-একটা school দাঁড়িয়ে যাচ্ছে বা অন্যান্য school-এর সঙ্গে মাথা ফাটাফাটি বাঁধছে এমন নয়। গণতন্ত্রের দেশের জনসাধারণ কোনো একজনকে অসাধারণ হতে দেয় না। আমেরিকা, ফ্রান্স ও রাশিয়ার চেয়েও ইংল্যাণ্ডের গণতন্ত্র খাঁটি। সেইজন্যে ইংল্যাণ্ডে একটি ফোর্ড বা আনাতোল ফ্রাঁস বা লেনিন সম্ভব হয় না।
তবে এটা কেবল ইংল্যাণ্ডের নয়, এ যুগের সব দেশেরই অবশ্যম্ভাবী দুর্ভাগ্য। গণতন্ত্রের সঙ্গে মহাপুরুষের খাপ খায় না। গণতন্ত্রের সব সুখ, কেবল ওই একটি দুঃখ। গণতন্ত্র সকলকে সমান করতে চায়, কাউকে অসমান করতে চায় না। আগে ছিল ভোটের সাম্য, এখন আসছে মজুরির সাম্য, তারপর আসবে মাথার সাম্য। স্কুলমাস্টারের সাহায্যে সকলের মাথাকে সমান শক্তিবিশিষ্ট না করলে বুদ্ধির জোরে গোটা কয়েক লোক বাকি সকলের চেয়ে সুবিধা করে নিতে পারে। এখন থেকেই কোনো কোনো লোক সোশ্যালিজমের বিরুদ্ধে এই বলে আপত্তি করছে যে, সকলকে যদি সব বিষয়ে সমান সুযোগ দেওয়া হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা ইহুদি বংশীয় তারাই বুদ্ধির জোরে বড়ো বড়ো পদগুলো দখল করবে বা বাকি সকলের ওপরে সর্দারি করবে। সব সইতে রাজি আছি, কিন্তু ইহুদির কর্তৃত্ব…। কিন্তু ইহুদিকে কোনো বিষয়ে কোনো সুযোগ না দিলেও কি তাকে দাবিয়ে রাখা যায়? ইহুদি যে শোলার মতো, তাকে সমুদ্রের তলে পাথরচাপা দিলেও সে ভাসবেই। ইউরোপ আমেরিকার এমন কোন দেশ আছে যেখানে ইহুদিকে হাজার দাবিয়ে রাখলেও সে উপরে ওঠেনি? ভাবী কালের গণতন্ত্রে রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, মুড়ি-মিছরি সকলেরই একদর হবে, কিন্তু কতগুলো লোক যদি বেশি বুদ্ধিমান হয় তারা তো বেশি সুবিধা করে নেবেই—তারা ইহুদি বা আর যা-ই হোক-না কেন। শেষকালে তাদের বংশবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, বংশধরদের মাথা সমান করতে হবে। রাশিয়ার মানুষের মাথাকে বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা করে তার উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা হচ্ছে, কিন্তু উৎকর্ষের তারতম্য থেকে গেলে তম-প্রত্যয়ান্ত মাথাগুলো তর-প্রত্যয়ান্তদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙতে চাইবে না কি?
এমন কথাও আজকাল শুনতে হয় যে, আর্টকে সকলের হাতে পৌঁছে দিতে হবে, দর্শনকে সর্বজনবোধ্য করতে হবে, সব শাস্ত্রের অ-আ-ক-খ সকলের জানা চাই, সকলেই একখানা করে মোটর গাড়ি পাবে, সকলের মাথায় bowler hat না থাকলে সর্বমানবের ঐক্যবোধ হবে না, সকলের গায়ে কটিবস্ত্র না থাকলে ভারতবর্ষের মধ্যে ধনী-দরিদ্র ভেদ থেকে যাবে। গণতন্ত্রের যুগের যতগুলি প্রোফেট সকলেই সাম্যবাদী এবং সাম্য বললে এ যুগে বোঝায় বহিঃসাম্য। গান্ধী, লেনিন, ফোর্ড, বার্নার্ড শ প্রত্যেকেই নিজ নিজ ইউটোপিয়ায় সব মানুষকে সমান বানাতে চান। কিন্তু সব মানুষ কি আত্মায় সমান নয়, কোনোদিন সমান ছিল না? সব মানুষ কি দেহে মনে সমান হতে পারে, কোনোদিন সমান হবে? অতীতে আমরা অধিকারী ভেদের উপরে বড়ো বেশি জোর দিয়েছিলুম, বর্তমানে আমরা অধিকারী সাম্যের উপরে বড়ো বেশি জোর দিচ্ছি। সেইজন্যে আমাদের মধ্যে যাঁরা আর্টিস্ট তাঁরা ভাবছেন যে-আর্ট জন কয়েক সমঝদারের মধ্যে নিবদ্ধ, সে-আর্ট একটা মহার্ঘ বিলাসিতা। আর্টকে জনসাধারণের যোগ্য করতে গিয়ে দুধের সঙ্গে জল মেশাতে হবে। যাঁরা উদ্ভাবক তাঁরা এমন মোটর গাড়ি উদ্ভাবন করতেই ব্যস্ত যে মোটর গাড়ি সবচেয়ে সস্তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো হবে, তা নইলে বেশি লোকে মোটর কেনবার সুখ থেকে বঞ্চিত হবে। যাঁরা শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞ তাঁদের ইচ্ছা শিক্ষাকে এমন সুকর করা যাতে বহুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী স্বল্পতম সময়ে বহু বিষয়ে শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারবে। ইংল্যাণ্ডে দেখছি ছেলে-মেয়েদের মধ্যে এক শ্রেণির বই বাজার ছেয়ে ফেলেছে। ‘Children, do you know?’ এই হল প্রশ্ন। এর উত্তর বইয়ের পাতায়। কে সর্বপ্রথম কিলিমাঞ্জারো পাহাড়ের চূড়ায় হাতি দেখেছিল, কোথায় গাছের ডালে বিছানা পেতে মানুষেরা শোয়, কোন তারাটার আলো পৃথিবীতে পৌঁছোতে ঠিক বারো বছর এগারো মাস উনত্রিশ দিন তেইশ ঘণ্টা লাগে—এমনই সব উদ্ভট প্রশ্নের উত্তর না জেনে রাখলে ভদ্রসমাজে বেচারা শিশু পন্ডিত বলে মুখ দেখাতে পারবে না, প্রতি প্রশ্নে অপদস্থ হবে।
সব জিনিস যে সকলকে জানতেই হবে পেতেই হবে করতেই হবে এইটে আমাদের যুগের কুসংস্কার। এরই উৎপাতে আমরা গভীরতার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে প্রসারের দিকেই দৃষ্টি দিচ্ছি বেশি। একটা তাজমহল সৃষ্টি না করে এক লাখ বাসগৃহ তৈরি করছি। একটি যিশুর জন্যে প্রস্তুত না হয়ে সহস্র সহস্র পাদরি প্রস্তুত করছি। Mass production-এর পেছনেও এই মনোভাব। দু-একজন কোটিপতির ভোগের জন্যে নির্মিত একটি ময়ূর সিংহাসন এ যুগে অসম্ভব, এ যুগের শিল্পীদের চোখ public-এর ভোগযোগ্য একরাশ এক প্যাটার্নে তৈরি লোহার বেঞ্চির উপরে, যে-বেঞ্চিতে বসে একজন কয়লা ফেরিওয়ালা এক পেনি দামের Daily Mail পড়তে পড়তে বিশ্রাম করবে। রাশিয়ার রাজপ্রাসাদগুলো এখন নাকি গুদামঘরে পরিণত হয়েছে, Versailles-এর রাজনগর এখন একটা চিত্র প্রদর্শনী। আভিজাত্যের ভাবটা পর্যন্ত লোপ পেয়ে যাচ্ছে। যারা লোপ পেতে দিচ্ছে তারা আর কেউ নয়, অভিজাতেরা স্বয়ং। রুমানিয়ার রানি এক পেনি দামের খবরের কাগজের জন্যে নিজের ঘরোয়া সুখ-দুঃখের কাহিনি লিখে প্রচুর টাকা পান, তবে তাঁর ঠাট বজায় রয়! লর্ডেরাও কেউ মদ বিক্রি করে লাখপতি হবার পরে লর্ড পদবি পেয়েছেন। কেউ জাহাজের খালাসিগিরি করবার পরে ওকালতিতে উন্নতি করে লর্ড পদবি পেয়েছেন। ইংল্যাণ্ডে তবু নামমাত্র একটা লর্ড শ্রেণি আছে; ফ্রান্স জার্মানি প্রভৃতি দেশে বুর্জোয়ারাই সর্বোচ্চ শ্রেণি এবং রাশিয়াতে সে-শ্রেণিও নেই।
একদিন মানুষ প্রাণপণে যা চায় আরেক দিন যখন হাতের মুঠোয় তা পায় তখন ভাববার সময় আসে যা পেলুম সত্যিই কি তা এতই ভালো যে এরজন্যে যা হাতে ছিল তাকে ছাড়লুম! ইউরোপের কেউ কেউ এখন ভাবতে আরম্ভ করেছেন, গণতন্ত্র কি অভিজাততন্ত্রের চেয়ে সত্যিই ভালো? লাখ লাখ মাঝারি মানুষ কি এক-আধ জন মহাপুরুষের চেয়ে সত্যিই কাম্য? The greatest good of the greatest number কি প্রতি মানুষকে একটি করে ভোট ও একশো টাকা করে মাইনে দিলে হয়? খাওয়া পরার কষ্ট ও পরাধীনতার কষ্ট অতি অসহ্য কষ্ট, কিন্তু এ কষ্ট দূর করলেও কি সবচেয়ে বড়ো কষ্টটা থাকবে না? সবচেয়ে বড়ো কষ্ট কোয়ালিটির অভাব। দু-একটি মানুষ যদি বাকি সকলের চেয়ে অত্যন্ত বেশি বড়ো হয় তবে সেই অত্যন্ত বেশি বড়ো হওয়াটা কি বাকি সকলের পক্ষে greatest good নয়? ক্যাপিটালিজমের পেছনেও একপ্রকার আভিজাত্য ছিল। এক এক জন ক্যাপিটালিস্ট যখন পৃথিবীব্যাপী ব্যবসা ফাঁদেন, প্রকান্ড একটা combine-এর কর্তা হন, তখন তাঁর সেই শ্রেষ্ঠতা কি মানবজাতির শ্রেষ্ঠতা নয়? কিন্তু ইংল্যাণ্ডের মতো দেশে ক্যাপিটালিজমের দৌড় সীমাবদ্ধ হয়ে এসেছে, আমেরিকাতেও হয়ে আসবে। ক্যাপিটালিজম থামবেই, কিন্তু যে-বুদ্ধিবলের আভিজাত্য ক্যাপিটালিজমের পেছনে, সেই আভিজাত্যও যদি সেইসঙ্গে থামে তবে তাতে মানুষের লাভ বেশি না ক্ষতি বেশি?
আমেরিকার স্বাধীনতা, ফ্রান্সের বিপ্লব ও ইংল্যাণ্ডের যান্ত্রিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যে-সাম্যবাদ জড়িত ছিল সে-সাম্যবাদ সমস্ত পৃথিবীকে সমতল না করে ছাড়বে না। এই দেড় শতাব্দীর মধ্যে সে ইউরোপ আমেরিকাকে একাকার করে তুলেছে। এখন এক স্থানে বসেই দেশভ্রমণের ফল পাওয়া যায়। ইতর ভদ্র শূদ্র ব্রাহ্মণ শ্রমিক ধনিক প্রজা রাজা নারী নর তরুণ প্রবীণ সকলকেই এক নেশায় পেয়েছে—পরস্পরের সমান হতে হবে। এ যুগের একমাত্র বিরোধী সুর কেবল নিটশে। কিন্তু তাঁর চেলারা তাঁর পরুষকন্ঠকে যথেষ্ট ললিত করতে লেগেছেন, তা নইলে ডেমোক্রেসির কর্ণপটহে ব্যথা লাগবে। আসল কথা বৈষম্যবাদের সবে শুরু হচ্ছে। অসম পুরুষকে ঠিকমতো কল্পনা করতে পারা যাচ্ছে না। কল্পনা করেও কোনো ফল নেই। তিনি যখন আসবেন তখন আপনি আসবেন, তাঁকে বানাবার ভার যে-বামনরা নিতে চায় তাদের সব কল্পনার চেয়ে তিনি বড়ো। তিনি এলে তাঁর সমাজের যে কেমন চেহারা হবে তার নকশা তৈরি করা এইচ জি ওয়েলসেরও অসাধ্য।
১১
সম্প্রতি এখানে air raid হয়ে গেল। একদল লোক এরোপ্লেনে লণ্ডন আক্রমণ করলে, আরেক দল লোক লণ্ডন রক্ষা করলে। যুদ্ধটা এমন নিঃশব্দে হল যে খবরের কাগজ ছাড়া কোথাও রেশ রেখে গেল না। নিন্দুকেরা বলছে আসল যুদ্ধ এত সহজ ব্যাপার নয় এবং যারা সত্যিই লণ্ডন আক্রমণ করবে তারা এই যাত্রার দলের যোদ্ধাদের রিহার্সালের সুযোগ দেবে না।
ইংল্যাণ্ডের মতো দেশে যুদ্ধ একটা নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম। যারা পেশাদার সৈনিক তারা ভাবী যুদ্ধের জন্যে প্রতিদিন প্রস্তুত রয়েছে, যারা অব্যবসায়ী তারাও ‘দরকার পড়লে সৈনিক হব’ এই মনোভাব নিয়ে খাটছে ও খেলছে। এক্ষেত্রে বড়োলোক ছোটোলোক নেই, সব শ্রেণির সব অবস্থার লোকের পক্ষে এটা সন্ধ্যাহ্নিকের মতো আচরণীয়। পাঁচ বছরের ছেলের দলও মার্চ করে বাজনা বাজিয়ে শোভাযাত্রায় চলে, বড়োদের তো কথাই নেই। মেয়েরা তাদের নকল করে উৎসাহ দেয় এবং নিজেরা দল করে যুদ্ধের আনুষঙ্গিক ক্রিয়াগুলোর জন্যে তৈরি হয়। আহতদের শ্রুশ্রূষার ভার তো মেয়েদেরই উপরে। আকাশ-যোদ্ধাদের মধ্যে মেয়েও আছে।
সামরিক সংস্কার এদের আবালবৃদ্ধবনিতার মজ্জাগত। পরিবারে দুটি-একটি ছেলে যুদ্ধকে তাদের জীবিকা করবেই, একথা প্রত্যেক পিতা-মাতা একরকম ধরেই রাখেন এবং পরিবারের দুটি-একটি মেয়ে সৈনিককে বিবাহ করে বিধবা হলেও হতে পারে, এও পিতা-মাতার দূরদৃষ্টির বাইরে নয়। একান্নবর্তী পরিবার এদেশে নেই, ছেলে বড়ো হলে ঘর ছেড়ে যায়, তার উপরে বাপ-মায়ের দাবি নগণ্য। সুতরাং ছেলে যদি যুদ্ধে প্রাণ হারায় তবে বাপ-মায়ের শোক যত বড়োই হোক অসুবিধা অপ্রত্যাশিত হয় না। একান্নবর্তী পরিবার প্রথা না থাকায় এদেশের যুবকদের পক্ষে দুঃসাহসিক কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের তুলনায় সহজ। বিধবাবিবাহও এদেশে নিষিদ্ধ নয়, সুতরাং স্বামী যুদ্ধে প্রাণ দিলে স্ত্রীর শোক যত বড়োই হোক আশার ক্ষীণ রশ্মি থাকে। সেইজন্যে হয় প্রাণ দিতে নয় যশস্বী হতে এদের স্ত্রীরা যেমন এদের যুদ্ধে ঠেলে, আমাদের স্ত্রীরা তেমনি আমাদের যুদ্ধে দূরের কথা—বিদেশে যেতেও ঠেলে না, অধিকন্তু বাধা দেয়! যখন সহমরণ প্রথা ছিল তখন স্ত্রীর আনুকূল্য পাওয়া দুষ্কর ছিল না, কেননা বৈধব্যের যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতির উপায় ছিল; এবং পুনর্মিলনের আশাও ছিল নিকট।
আমাদের স্ত্রীলোকদের মতো প্রচ্ছন্ন শত্রু আমাদের আর নেই। তারা যে এদের স্ত্রীলোকদের চেয়ে স্নেহময়ী এমন মনে করলে দেশকাল-নিরপেক্ষ নারীপ্রকৃতির প্রতি অবিচার করা হয়। কিন্তু তারা এদের স্ত্রীলোকদের তুলনায় স্নেহান্ধ, তারা আমাদের ‘রেখেছে বাঙালি করে, মানুষ করেনি।’ কোনো দুঃসাহসিক ব্রতে তারা আমাদের নিষ্ঠুর আনুকূল্য করে না, তাই সে হতভাগিনীদের আমরা ‘পথি বিবর্জিতা’ করে সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়াটাকেই মনে করি চরম দুঃসাহসিকতা। এবং যখন সন্ন্যাসী হয়ে যাই, তখন কুলবনিতায় বারবনিতায় ভেদ রাখিনে, এক নিশ্বাসে বলে যাই নারী কালভুজঙ্গিনি, কামিনীকাঞ্চনের সঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। ইউরোপের উপরে যে-খ্রিস্টিয়ানিটি নামক সন্ন্যাসীশাসিত ধর্মমতটি চাপানো হয়েছে সেটিও সম্ভবত বৃহৎ পরিবার-কণ্টকিত কাঁটা গাছের ফল। কিন্তু খ্রিস্টিয়ানিটি তো ইউরোপের সত্যিকার ধর্ম নয়, সরকারি ধর্ম। তাই চার্চের কর্তারাও স্টেটের কর্তাদের মতো যুদ্ধবিগ্রহে পান্ডার কাজ করে থাকেন। এমনকী ফরাসি যাজকরা উঁচু দরের ডিপ্লোম্যাট ও পোর্তুগিজ যাজকরা উঁচু দরের ব্যবসাদারও হয়ে থাকেন। এই যে এখন যুদ্ধ নিবারণের প্রচেষ্টা চলেছে, এতে চার্চের নেতৃত্ব নেই, এবং যেটুকু যোগ আছে সেটুকু চার্চভুক্ত জন কয়েক ব্যক্তি-বিশেষের।
ইংল্যাণ্ডে যুদ্ধবিরোধী শান্তিবাদীর সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু যে-কারণে বাড়ছে সে-কারণটা ইংল্যাণ্ডের বার্ধক্যের লক্ষণ কি না বলা যায় না। শান্তিবাদীদের দলে যাঁদের নাম দেখি তাঁরা সাধারণত বর্ষীয়ান এবং তাঁদের ভাবনা এই যে, আধুনিক যুদ্ধপ্রক্রিয়াকে যদি একটুও প্রশ্রয় দেওয়া যায় তবে ভাবী যুদ্ধে সমস্ত পৃথিবী ছারখার হয়ে যাবে। এরোপ্লেন থেকে বোমা ছুড়ে এক শতাব্দীর এত বড়ো লণ্ডন শহরটাকে এক দিনেই শ্মশান করে দেওয়া সম্ভব। মানুষ যত সহজে ধ্বংস করতে শিখেছে তত সহজে নির্মাণ করতে শেখেনি। একটা যুদ্ধের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে কত বৎসর চলে যায়। আধুনিক যুদ্ধ প্রক্রিয়া এমন মারাত্মক যে, যেসব দেশ যুদ্ধে যোগ দেবে না সেসব দেশেও মহামারি পৌঁছোতে পারবে। এবং এক দেশের বিষে সব দেশ জর্জর হতে পারবে। এক জাতির ক্ষতিতে সব জাতির ক্ষয়, এটা যে কত বড়ো সত্য তা মানুষ এতকাল বুঝত না, এখন বুঝছে। কিন্তু বুঝলে কী হয়, বুদ্ধি তো মানুষের সব নয়, প্রবৃত্তি যে তার বুদ্ধির অবাধ্য। ‘জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।’ গত মহাযুদ্ধে যে-শিক্ষাটা হল, সে-শিক্ষা ইতিমধ্যেই বাসি হয়ে গেছে। আর কয়েক বছরেই নতুন জেনারেশন রাজত্ব করবে; নবীন চিরদিনই বেপরোয়া; শৈশবের যুদ্ধস্মৃতি যৌবনে মিলিয়ে যাবে; তখন চলবে নতুন যুদ্ধে নতুন কীর্তির আয়োজন। সে-আয়োজনে তরুণকে প্রেরণা দেবে তরুণী; সে তার কানে কানে বলবে, ‘None but the brave deserves the fair’; অর্জুনের রথে সারথি হবে সুভদ্রা। তারপরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। তারপরে পতি-পুত্রহীনাদের নারীপর্ব; তারপরে আবার নতুন বংশ, নতুন পুরুষ, নতুন সৃষ্টি।
বেঁচে থেকে মানুষ করবে কী? মানুষ যে কঠিন কিছু না করতে পারলে জড় হয়ে যায়, ভীরু হয়ে যায়। যুদ্ধ মানুষ হাজার হাজার বছর করে আসছে শুধু কঠিন কিছু না করে তার শান্তি নেই বলে। যুদ্ধহীন জগতের শান্তির মতো অশান্তি তার পক্ষে আর নেই। মানুষ যে মানুষকে হিংসাই করে এটা মিথ্যা, সুতরাং ‘অহিংসা পরমো ধর্মঃ’ মানুষের পরম ধর্ম নয়। মানুষ আঘাত করতে ও আঘাত পেতে ভালোবাসে, কারণ মানুষ প্রেমিক। তার প্রেমে আঘাত আছে, অবহেলা নেই। অহিংসা তো অবহেলারই নামান্তর। আমি তোমাকে অহিংসা করি বললে তোমার প্রতি কিছুই করা হয় না, না ভালো না মন্দ। অহিংসা হচ্ছে একলা মানুষের নিষ্ক্রিয় মানুষের ধর্ম, সে-মানুষ অসহযোগীই বটে। তেমন মানুষের সমাজে বাস করে আনন্দ নেই। আমরা চাই দুটো মারতে দুটো মার খেতে, আমরা রাগীও বটে অনুরাগীও বটে, কিন্তু রক্ষা করো, আমরা বৈরাগী নই।
আধুনিক যুদ্ধ প্রক্রিয়ায় মানুষকে কি মানুষের নিকট করে তোলেনি? মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলায়নি? অধিকাংশ মানুষ দেশের বাইরে যাওয়ার সুযোগ পায় না প্রধানত আর্থিক কারণে। যুদ্ধের সময় সৈন্যদলে যোগ দিয়ে তারা যখন বিদেশ অভিযান করে তখন বিদেশকে জানবার সুযোগ পায়, বিদেশিকেও জানে। গত মহাযুদ্ধে দ্বীপবদ্ধ ইংরেজ প্রথম বার জার্মান সংস্পর্শে এসে জার্মান জাতিকে জানল, তার ফলে এখন জার্মানির প্রতি শ্রদ্ধা তাদের কত! গত মহাযুদ্ধে ফ্রান্স থেকে যাঁরা যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন তাঁদের কারো কারো লেখায় পড়লুম, জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণেই দুই যোদ্ধা বোঝে যে তারা দুজনেই মানুষ, তাদের দুজনের কিছুমাত্র বিরোধ নেই। কীসের এক অবোধ্য প্রেরণায় তাদের একক্ষেত্রে মিলিয়েছে; অমূল্য এ মিলন, কিন্তু এর মূল্য দিতে হবে জীবনদান করে। মিলন মাত্রেই বিয়োগান্ত!
ভাবী যুদ্ধের বিশ্বব্যাপী মহামারিতে মানুষকে আরেকটুখানি মিলাবে। অকথ্য লোকসান দিয়ে মানুষ জানবে যে, সকলেরই স্থান এক নৌকায়। ভারতবর্ষের লোক ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে এসে দেখে গেছে পৃথিবীটা নেহাত ছোটো, ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগে মেনে নিয়েছে পৃথিবীর এক কোণের ছোঁয়াচ আরেক কোণে পৌঁছায়। গত মহাযুদ্ধের পর সকলেই অল্পাধিক বুঝেছে যে, জেলায় জেলায় যুদ্ধ যেমন জ্ঞাতিবিরোধ, দেশে দেশে যুদ্ধও তেমনি জ্ঞাতিবিরোধ। সেদিন এক গির্জার দ্বারে লিখেছে :
Duelling is illegal. War is the duel between nations. Why not make it illegal by taking your national quarrel to an international court of justice?
এদেশের ‘লিগ অব নেশনস ইউনিয়ন’ যুদ্ধনিবারণের জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে। নানা দেশের নানা জাতির মানুষের যাতে দেখাশুনো আলাপ পরিচয় হয় সে-চেষ্টারও বিরাম নেই। ভাবী যুদ্ধ যদি নিকট ভবিষ্যতে ঘটে তবে ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণ আত্মরক্ষারগুরুতর কারণ না দেখলে যুদ্ধে নামতে চাইবে কি না সন্দেহ। যদি সুদূর ভবিষ্যতে ঘটে তবে বুদ্ধির চেয়ে প্রবৃত্তিই প্রবল হবে বোধ হয়। পৃথিবীকে এক রাষ্ট্রে পরিণত না করা অবধি যুদ্ধের ক্ষান্তি নেই। শুধু এক রাষ্ট্র নয়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। শুধু গণতান্ত্রিক নয়, ধনসাম্যমূলক। রেল স্টিমার যেমন কলকাতা, বম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লিকে পরস্পরের পক্ষে নিকটতর করে ভারতবর্ষকে এক রাষ্ট্র করেছে, এরোপ্লেন তেমনি নিউ ইয়র্ক, লণ্ডন, কায়রো, সিঙ্গাপুর, টোকিওকে পরস্পরের পক্ষে নিকটতর না করা অবধি পৃথিবীব্যাপী এক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশা নেই। তবে ইউরোপ যে তাড়াতাড়ি এক রাষ্ট্র হয়ে উঠছে এর সন্দেহ নেই। ‘United States of Europe’ আর বেশি দিন নয়, পঞ্চাশ বছর।
যুদ্ধ যদি উঠে যায় তবে যুদ্ধেরই মতো কঠিন কিছু উদ্ভাবন করতে হবে। নতুবা মৃত্যুসংখ্যা কমাবার জন্যেই যদি যুদ্ধ তুলে দিতে হয় তবে বৃদ্ধের সংখ্যা বেড়ে যাবে; সমগ্র পৃথিবীটাই একটা ভারতবর্ষ হয়ে উঠবে, যেখানে যযাতির রাজত্ব হাজার কয়েক বছর থেকে চলে আসছে। তখন পৃথিবীময় ‘পিতা স্বর্গ’ ও ‘জননী স্বর্গাদপি’র জ্বালায় মাথাটা ভক্তিতে এমন নুয়ে আসবে যে মেরুদন্ড যাবে বেঁকে, এবং পিঠের উপর চেপে বসবেন পতিব্রতার দল। ইউরোপেরও যদি এহেন অবস্থা হয়, তবে পৃথিবীর কোথাও বাস করে শান্তি থাকবে না, সর্বত্রই এত শান্তি! যুদ্ধ যদি উঠে যায় তবে যৌবনের পক্ষে সে বড়ো দুর্দিন। ভাবুকরা বলছেন প্রচুর খেলাধুলার ব্যবস্থা করা যাবে, ভয় নেই। এই যেমন Olympic games। কিন্তু এও যথেষ্ট নয়। এমন কিছু চাই যা আরও বিপজ্জনক, আরও প্রাণান্তক। সমাজকে অতীত কালের মতো ভাবীকালেও প্রচুর প্রাণক্ষয় করে প্রচন্ড প্রাণশক্তির পরিচয় পেতে হবে, সমাজের বাজেটে লোকসানের ঘরের অঙ্ক চিরকাল সমান বিপুল হওয়া চাই। ইতিহাসে এই দেখা গেছে যে, কোটি প্রাণীর তপস্যায় কয়েকটি প্রাণী সিদ্ধিলাভ করেছে, অভিব্যক্তির ইতিহাসে যোগ্যতমেরই উদবর্তন। যে-মানুষ সাহসে উদ্যমে উদ্যোগে বিক্রমে যোগ্যতম, সে-মানুষকে সহজ পথ দেখিয়ে মানবজাতি লাভবান হবে না।
যুদ্ধকে অনাবশ্যক বলে যদি তুলে দেওয়া হয় তো ভালোই, কিন্তু ক্ষতিকর বলে যদি তুলে দেওয়া হয় তবে বুঝতে হবে ক্ষতি স্বীকার করবার মতো ক্ষমতা মানবজাতির নেই। সে ক্ষমতা বর্বরের ছিল, কেননা বর্বরের প্রাণশক্তি ছিল প্রভূত। সভ্যতা যদি মানবের প্রাণশক্তি হরণ করে থাকে তবে সভ্যতার পক্ষে সেটা ভয়ের কথা। বর্বরতার শক্ত বনিয়াদের উপরে প্রতিষ্ঠিত না-হলে সভ্যতার পাকা দালানে ফাটল দেখা দেয়। মানবের মধ্যে যে-পশু আছে তাকে দুর্বল করলে মানব দুর্বলই হয়। বহুকাল মানবকে মনে করা হয়েছে পশু থেকে স্বতন্ত্র একটা সৃষ্টি, একেবারে ভুঁইফোঁড়। সভ্য মানবকে মনে করা হয়েছে বর্বর থেকে স্বতন্ত্র একটা জাতি, পূর্বপুরুষহীন। কৌলীন্যের পেছনে যেন সাংকর্ষ নেই, আভিজাত্যের পেছনে যেন জারজতা নেই, পদ্মের পেছনে যেন পাঁক নেই! আসলে কিন্তু পাঁকই হচ্ছে সার, সে না থাকলে জলের পদ্ম হত কাগজের পদ্ম। বহুকাল থেকে আমরা বর্বরতার তেজ হারিয়ে সভ্যতার আলো নিয়ে খেলা করে এসেছি, তৈমুরের ভোঁতা তরোয়ালে শান দিয়ে তাকে দাড়ি চাঁচবার ক্ষুর বানিয়েছি, জীবনের মোটা কথাগুলোর সূত্র হারিয়ে সূক্ষ্ম তত্ত্বের জট পাকিয়েছি।
সেইজন্যে দেখি আমাদের যুগে আদিম যুগের সঙ্গে অন্বয়রক্ষার চেষ্টা; কেউ বলছে ‘back to the village’; কেউ বলছে ‘back to the forest’; কেউ বলছে বর্বরের মতো দিগম্বর হও; কেউ বলছে পশুর মতো আকাশের তলে ঘাসের উপরে খাও-শোও। এসবের তাৎপর্য এই যে, আমরা আদিম প্রাণীর জোর হারিয়েছি, আপনার গাঁথা জালে জড়িয়েছি। অতিবুদ্ধির নাকে দড়ি; সেই হয়েছে সভ্যমানবের দশা। যুদ্ধ দোষের নয়, দোষের হচ্ছে কূটনীতি, গুপ্তচরবৃত্তি, বিষবায়ু প্রয়োগ, ব্যাধিবীজ বিক্ষেপ ইত্যাদি কৌরবসুলভ কুকার্য। মানুষ ধর্মযুদ্ধ ভালোবাসে, সে-যুদ্ধে তার গুণাগুণের পরিচয় দিয়ে সে তৃপ্তি পায় মরণেও। কিন্তু আধুনিক যুদ্ধের বারো আনাই যে মিথ্যাপ্রচার, কাগজে কাগজে যুদ্ধ। অসির চেয়ে মসির উপদ্রব বেশি। আধুনিক যুদ্ধে যত মানুষ প্রাণে মরে তার বেশি মানুষ আত্মায় মরে; এইখানেই অধর্ম—যুদ্ধে অধর্ম নেই।
যুদ্ধ একটা উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষমতার পরীক্ষা। যুদ্ধের চেয়ে সহজ উপলক্ষ্য চাইনে, যুদ্ধের পরিবর্তে অন্যবিধ উপলক্ষ্যে আপত্তি নেই। কিন্তু সে-উপলক্ষ্য যেন আবালবৃদ্ধবনিতাকে যেকোনো মুহূর্তে প্রাণ দিয়ে দিতে প্রস্তুত রাখে, সাহসে উদ্যমে উদ্যোগে বিক্রমে প্রত্যেককে ভরে দেয়। যুদ্ধনিবারণী প্রচেষ্টার যাঁরা নায়ক তাঁরা যুদ্ধের বদলে করবার কী আছে তা বলেননি, শুধু বলেছেন, ‘যুদ্ধ কোরো না’; হাঁ-মন্ত্র না দিয়ে দিচ্ছেন না-মন্ত্র; ‘Thou shalt’ না বলে বলছেন ‘Thou shalt not’। যুবকের প্রাণ ভাবের বদলে অভাবে ভরে ওঠে না, যুবক চায় positive commandment। যুদ্ধের বদলে সালিশি করা তরুণের কাজ নয় এবং যুদ্ধের বদলে পুলিশি করেও তরুণের তৃপ্তি নেই। তাই শান্তিবাদীদের আবেদন তরুণের বুক দোলায় না। এখন যদি কেউ এসে বলতেন ‘তোমরা প্রেমের অভিযানে জগতের হৃদয় জিনে নাও’ তবে সেও হত একরকম যুদ্ধ, তাতে দুঃখ কিছুমাত্র কম হত না, মরণাধিক বেদনা থাকত। সে-যুদ্ধে স্বার্থপরতার গ্লানি ও মিথ্যাভাষণের পাপ চাপা পড়ত এবং ভীরুতার স্থান থাকত না। সে-যুদ্ধে বর্বরকে ঘৃণা করে তার অবদান হতে সভ্যতাকে বঞ্চিত করা হত না; পশুকে অবহেলা করে তার সংস্পর্শ হতে মানুষকে দূরে রাখা হত না। যে-ডাক শুচি-বাতিকগ্রস্তের নয়, নীতি-বাতিকগ্রস্তের নয়, অহিংসা-বাতিকগ্রস্তের নয়, প্রেমিকের—সেই মারাত্মক ডাকের প্রতীক্ষায় আমাদের যুগ পদচারণ করছে।
১২
বসন্ত যখন আসে তখন এমনি করেই আসে। তখন ফুল যত ফোটে কুঁড়ি ঝরে যায় তার বেশি, যত ফুল সফল হয় তার বেশি ফুল হয় নিষ্ফল। ‘বসন্ত কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে? দেখিস নে কি শুকনো পাতা ঝরা ফুলের খেলা রে।’ লাভের চেয়ে লোকসানই বেশি; তবু অপরিসীম লাভ, সেই অপরিসীমতাকে বলি বসন্ত। জীবনের চেয়ে জরা-ব্যাধি-মৃত্যুই বেশি; তবু অপরিসীম জীবন, সেই অপরিসীমতাকে বলি যৌবন।
জার্মানিতে এসে দেখতে পাচ্ছি জাতির জীবনে বসন্ত এসেছে। জার্মানদের দেখে বিশ্বাস হয় না যে, কিছুদিন আগে এরা যুদ্ধে হেরে সর্বস্বান্ত হয়েছে এবং এখনও এরা অংশত পরাধীন ও অত্যন্ত ঋণগ্রস্ত। মুখে হাসি নেই এমন মানুষ আছে কি না খোঁজ নিতে হয়, এবং সকলেরই স্বাস্থ্য অনবদ্য। অথচ যুদ্ধে এরা প্রত্যেকেই ধন জন হারিয়েছে এবং মার্ক মুদ্রার পতনকালে এদের অধিকাংশের সর্বস্ব গেছে। কিন্তু সর্বস্ব গেলেও যদি যৌবন থাকে তবে সর্বস্ব ফিরে আসতে বিলম্ব হয় না। জার্মানির লোক ধন দিয়েছে, প্রাণ দিয়েছে, কিন্তু যৌবন দেয়নি। তাই এমন অবিশ্রান্ত যৌবনচর্চা চলেছে ক্ষতিকে পুষিয়ে নিতে। যারা গেছে তাদের স্থান পূরণ করছে যারা এসেছে তারা, শিল্প বিজ্ঞানে ক্রীড়ায় কৌতুকে নবীন জার্মানির পরাক্রম দেখে মনে হয় না যে প্রবীণ জার্মানি বেঁচে থাকলে এর বেশি পরাক্রমী হতে পারত।
বসন্তকে যেমন কুঁড়ি ঝরাতে হয় লাখে লাখে, সমাজকে তেমনি মানুষ খোয়াতে হয় লাখে লাখে। প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের শর্ত এই যে, প্রকৃতি আমাদের যা দেবে তা আমরা পালা করে ভোগ করব। আমাদের এক দলকে মরতে হবে আরেক দলকে বাঁচতে দেবার জন্যে। মৃত্যুর মধ্যে যে-তত্ত্ব আছে সে আর কিছু নয়, সে এই—যারা জন্মায়নি তাদেরকে স্থান ছেড়ে দেবার জন্যে যারা জন্মিয়েছে তারা মরবে। সমাজকে তাই হয় দুর্ভিক্ষের জন্যে নয় যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হয়—দুর্ভিক্ষের মরা তিলে তিলে, যুদ্ধের মরা এক নিমেষে।* দুর্ভিক্ষে যারা মরে তারা আগে থাকতে দুর্বল, তারা সাধারণত বৃদ্ধ কিংবা শিশু কিংবা স্ত্রীলোক। আর যুদ্ধে যারা মরে তারা যুবা, সবচেয়ে বলবান, সবচেয়ে স্বাস্থ্যবান পুরুষ। যে-সমাজের যৌবন অফুরন্ত সে-সমাজ যুবাকেই মরতে পাঠায় যুবাকে স্থান ছেড়ে দেওয়ার জন্যে, সে-সমাজ কোনোদিন যুবার অভাববোধ করে না। আর সে-সমাজের যৌবন অল্প তার ব্যবস্থা অন্যরকম, যে-সমাজের যৌবন শুকিয়ে শুকিয়ে লোলচর্ম হলে পরে যখন তার মৃত্যু আসে তখন এক স্থবিরের স্থান পূরণ করতে থুড়থুড় করে অগ্রসর হয় আরেক স্থবির—ঠাকুরদা মশায়ের পরে জ্যাঠামশায়, তাঁর পরে বাবামশায়, তাঁর পরে কাকামশায়, তাঁর পরে দাদা, তার পরে আমি। চুল না পাকলে রাজত্ব করবার অধিকার কারুর নেই। সুতরাং বাল্যকাল থেকেই বার্ধক্যচর্চা করতে হয়।
কিন্তু ইউরোপে দেখছি বিপরীত ব্যাপার। যৌবনরক্ষা করবার জন্যে মহাস্থবিরেরা monkey gland-এর শরণ নিচ্ছেন, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ারা বালক-বালিকার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খালি গায়ে খোলা জায়গায় সাঁতার কাটছেন, নৌকা চালাচ্ছেন, কঠিন কাঠের তক্তারউপরে পড়ে পড়ে মধ্যাহ্নসূর্যের কিরণে সিদ্ধ হচ্ছেন। এটাও একটা ফ্যাশন, কিন্তু ফ্যাশন তো weather cock-এর মতো দেখিয়ে দেয় বাতাস কোন দিক থেকে বইছে। যুদ্ধের আগে জার্মানিতে প্রত্যেক পুরুষকেই রণশিক্ষা করতে হত। এখন তার উপায় নেই, কিন্তু সংস্কার যায় কোথায়? জার্মানদের বহুকালাগত আদর্শ—মানুষকে হতে হবে ‘blood and iron.’ পুরুষদের সঙ্গে এখন মেয়েরাও যোগ দিয়েছে, জাতীয় দুর্দশা স্মরণ করে কেউ তাদের বাধা দিতেও পারছে না। চার্চ একটু খুঁতখুঁত করেছিল। ওরা বললে, অমন করলে চার্চ মানব না। তখন চার্চ হাল ছেড়ে দিলে। জার্মানদের মতো গোঁড়া খ্রিস্টান জাতি নিতান্ত দায়ে না ঠেকলে এ অনাচার সহ্য করত না।
যারা যুদ্ধে প্রাণ দেয় তারা দেশের সবচেয়ে প্রাণবান পুরুষ। যারা বেঁচে থাকে তারা বালবৃদ্ধবনিতা। তবু তাদেরই ভিতর থেকে নতুন সৃষ্টির উদগম যখন হয় তখন অবাক হয়ে দেখি এ সৃষ্টিও আগেরই মতো পরাক্রান্ত। তখন মনে হয় একে পরাক্রান্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্যেই আগের সৃষ্টিকে ধ্বংস হতে হল। জীবনকে আমরা বলে থাকি লীলা, এরা বলে থাকে সংগ্রাম। একই কথা। কেননা লীলা যেমন নবনবোন্মেষ, সংগ্রামও তেমনি নূতন সৃষ্টির জন্যে পুরাতনের ধ্বংস। বহু শতাব্দী ধরে দেখা যাচ্ছে প্রতি জেনারেশনে ফ্রান্স একবার করে নিঃক্ষত্রিয় হয়, তার বলবান পুরুষেরা প্রাণ দেয়, তার সুন্দরী নারীরা nun হয়ে যায়। তবু ভষ্মের ভিতর থেকে আগুন জ্বলে ওঠে, নতুন ফ্রান্সের কীর্তি পুরাতন ফ্রান্সের গৌরব ম্লান করে দেয়। ‘হইলে হইতে পারিত’ কথাটা অক্ষম দেশের পক্ষে প্রযোজ্য, ফ্রান্সের পক্ষে নয়। ফ্রান্স যা হয়েছে তা-ই এত আশ্চর্য যে, এই হওয়াটার খাতিরে তার ‘হইলে হইতে পারা’টা চিরকালের মতো না হওয়া থেকে গেল। যা হতে পারতুম তা-ই যদি হতুম, তবে যা হয়েছি তা হতে পারতুম না। বাস্তবটা এমন শোচনীয় নয় যে সম্ভাব্যতার জন্য হাহুতাশ করব। স্বর্গ থাকলে মর্ত যদি না থাকে তবে চাইনে স্বর্গ।
মহাযুদ্ধের অশেষ ক্ষতিকে স্বপ্ন করে দিয়ে জার্মানি নতুন দিনের আলোয় নতুন করে বাঁচছে। তার ধনবল নেই, সৈন্যবল নেই, কিন্তু তার লক্ষ লক্ষ বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া যেরূপ উৎসাহ আগ্রহ ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে যৌবনচর্চা করছে তা দেখে মনে হয় ভাবীকালের জার্মান জাতিকে নিয়ে আবার বিপদ বাঁধবে। জার্মানি যা করছে তার কোথাও কিছু কাঁচা রাখছে না। পৃথিবীর যেখানে যে-বিষয়ে যে-বই প্রকাশিত হয় জার্মানি তার অনুবাদ করে পড়ে, ক্ষুদ্র শহরের ক্ষুদ্র দোকানেও আমি ভারতীয় আর্টের উপরে লেখা বৃহৎ বই এবং মহাত্মা গান্ধীর Young India-র অনুবাদ দেখলুম! তা বলে ভারতবর্ষের প্রতি জার্মানির পক্ষপাত নেই, Sigrid Undset-এর নূতনতম বইয়ের অনুবাদও সে-দোকানে ছিল এবং যে-বই অল্পদিন আগে লণ্ডনে প্রকাশিত হয়েছে সে-বই অনুবাদ করতে জার্মানির বিলম্ব হয়নি। জার্মানির ছোটো ছোটো শহরেও যেসব মিউজিয়াম আছে সেগুলিতে পৃথিবীর কোনো দেশ বাদ পড়েনি। জার্মানির শিক্ষাপ্রণালীর গুণে দেশের ইতরসাধারণ ও পৃথিবীর কোন দেশে কোন বিষয়ে কতটা উন্নতি হয়েছে সে-খবর রাখে। ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণ এমন সর্বজ্ঞ নয়।
কিন্তু আমাকে সবচেয়ে চমৎকৃত করেছে দুটি বিষয়। প্রথমত, জার্মানির যে ক-টি ছোটো ও বড়ো গ্রাম ও শহর দেখলুম সে ক-টিতে Slum নেই, বরং মজুরদের বাড়িগুলি আমাদের মধ্যবিত্তদের বাড়ির তুলনায় অনেক উপভোগ্য। জার্মানির গরিব লোকদের অবস্থা ইংল্যাণ্ডের গরিব লোকদের চেয়ে অনেক ভালো। জার্মানির জাতীয় দুর্দশার দিনে তার শক্তিকে অপচয় থেকে রক্ষা করেছে তার অন্তর্বিবাদের স্বল্পতা। তা ছাড়া জার্মানি প্রমাণ করে দিচ্ছে যে যন্ত্রসভ্যতার সঙ্গে Slum-এর কিছু সোদর সম্বন্ধ নেই। দ্বিতীয়ত, জার্মানির শ্লীলতাবোধ এমন বনেদি যে, কলকারখানার সঙ্গে কদর্যতাকে সে প্রশ্রয় দেয়নি। ফ্যাক্টরিগুলো যথাসম্ভব গ্রাম বা শহরের বাইরে। তাদের ছোঁয়াচ বাঁচাবার জন্যে গ্রাম ও শহরের চতুঃসীমায় বাগান করে দেওয়া হয়েছে কিংবা বাড়ির সঙ্গে একটি বাগান করতে দেওয়া হয়েছে। শ্রমিকরা যেসব বাড়িতে থাকে সেসব বাড়িরও সুন্দর গড়ন সুন্দর রং; কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য প্রত্যেকেরই আছে। হোটেল বা রেস্তরাঁর দেওয়ালেও ওয়ালপেপারের বদলে একপ্রকার আলপনা। স্টেট থেকে অপেরা হাউস ও থিয়েটার বানিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রত্যেক শহরে। গান-বাজনার একটি আবহাওয়া সর্বত্র বোধ করা যায়। ইংল্যাণ্ডের সাধারণ লোক বোবা-কালা, এবং সিনেমা দেখে দেখে তাদের চোখও গেছে। কিন্তু জার্মানির সকলেই গান-বাজনায় যোগ দেয়। আর জার্মানিতে ছবি আঁকার ঝোঁক নিয়ে যত লোক বেড়ায়, ফোটো তোলার বাতিক নিয়ে তত লোক বেড়ায় না।
বেড়ানোর নেশা পৃথিবীর দুটি জাতির আছে, আমেরিকান আর জার্মান। কিন্তু আমেরিকান যখন বেড়ায় তখন ভেসে ভেসে বেড়ায়; দিনের দু-চার ঘণ্টায় দুশো মাইল দেখে নিয়ে বাকি সময়টায় বার বার খায়-দায় নাচে খেলে। তারজন্যে সবচেয়ে দামি রেল, জাহাজ, সবচেয়ে আরামের মোটর কোচ, সবচেয়ে বড়ো হোটেল। ভ্রমণ করবার সময় যাতে সে বিশ্রামসুখ পায় সেই দিকেই তার দৃষ্টি। কিন্তু জার্মান যখন বেড়ায় তখন পায়ে হেঁটে বেড়ায়, ফোর্থ ক্লাস রেলগাড়িতে চড়ে, নিজের পিঠে বাঁধা ‘ruck sack’ থেকে কিছু ‘wurst’ বার করে খায়, সস্তা সরাইতে গিয়ে পেট ভরে এক ঘড়া সস্তা beer পান করে, বিশ্রাম করতে করতে ছবি আঁকে আর চলতে চলতে প্রাণ খুলে গান গায়। জার্মানি দেশটি আমাদের যেকোনো প্রদেশের চেয়ে বড়ো। তার উত্তরটা প্রোটেস্টান্টপ্রধান, দক্ষিণটা ক্যাথলিকপ্রধান। তার প্রত্যেক জেলার নিজস্ব ইতিহাস আছে, প্রত্যেক জেলাই ছিল স্বতন্ত্র। জার্মানিকে একটি ছোটো স্কেলের ভারতবর্ষ বলতে পারা যায়, তেমনি বহুধাবিভক্ত। তাই জার্মানরা চায় নিজেদের দেশেরও অলিতে-গলিতে ঘুরে নিজের দেশকে সমগ্রভাবে জানতে। তাদের বেড়ানোর নেশার পেছনে তাদের এই উদ্দেশ্যটি আছে। যুদ্ধে হেরে জার্মানি এক হয়েছে। আগে ছিল প্রাশিয়ার একাধিপত্য। তবু প্রাদেশিকতা সম্পূর্ণ মরেনি এবং প্রোটেস্টান্টে-ক্যাথলিকে বিরোধ আছে।
জার্মানরা ইংরেজদের মতো প্রধানত প্রোটেস্টান্ট বা ফরাসিদের মতো প্রধানত ক্যাথলিক নয়। এদের দুই সম্প্রদায়ই সমান প্রবল। রাইনল্যাণ্ড ও ব্যাভেরিয়ার সর্বত্র ক্যাথলিক প্রভাব লক্ষ করছি। গির্জার যেমন সংখ্যা নেই, তেমনি গির্জার বাইরে ও ভিতরে মূর্তি ও চিত্রেরও সংখ্যা নেই। এখনও লোকে সেসব প্রতিমার কাছে দীপ জ্বালে, ফুল রাখে, হাঁটু গাড়ে, মাথা নোয়ায়, মনস্কামনা জানায়। খ্রিস্টিয়ানিটি বহুদূর থেকে এলেও ইউরোপের হৃদয় অধিকার করেছে।
মূর্তি ও চিত্রগুলি সচরাচর ক্রুশবিদ্ধ যিশুর কিংবা যিশুজননী মেরির। যিশুর পবিত্র জন্ম ও করুণ মৃত্যু—এই দুটি বিষয় নিয়ে অসংখ্য চিত্রকর চিত্র এঁকেছেন, অসংখ্য ভাস্কর মূর্তি গড়েছেন এবং অসংখ্য সংগীতকার গান রচনা করেছেন। মধ্যযুগের ইউরোপীয় আর্ট প্রধানত এই দুটি বিষয়কে অবলম্বন করে আত্মপ্রকাশ করেছিল। রেনেসাঁসের পরে ইউরোপ নিজেকে চিনল, বিষয়ে দারিদ্র্য রইল না এবং ইউরোপীয় আর্ট গির্জার আঁচল ছাড়ল। খ্রিস্টিয়ানিটি যে ইউরোপের অন্তরের অন্তঃস্থলে পৌঁছায়নি তার প্রমাণ খ্রিস্টিয়ানিটিকে ইউরোপ আপন ইচ্ছামতো ভাঙতে-গড়তে পারেনি, যেমনটি পেয়েছিল তেমনটি রাখতে চেষ্টা করেছে। সুন্দর সামগ্রী উপহাররূপে পেলে লোকে সাজিয়ে রাখতেই ব্যস্ত হয়।
খ্রিস্টিয়ানিটিকে তার বাড়ির পাশের আরব পারস্যের লোক গ্রহণ করলে না; এমনকী তার বাড়ির লোক ইহুদিরা পর্যন্ত অসম্মান করলে, কিন্তু দূর থেকে ইউরোপ ডেকে নিয়ে মান দিল। কেন এমন ঘটল? সম্ভবত ইউরোপের পরিপূরকরূপে এশিয়াকে দরকার ছিল। কিংবা ইউরোপীয় চরিত্রের পরিপূরকরূপে যিশুর আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তটির প্রয়োজন ছিল। জার্মানির যেখানে যাই সেখানে দেখি যিশুর ক্রুশবিদ্ধ করুণ মূর্তিটি বাণবিদ্ধ পাখির মতো দুটি ডানা এলিয়ে মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়েছে, যেন বিনা কথায় বলতে চায়, ‘আমার দুঃখ দেখে কি তোমাদের মায়া হয় না? তোমরা এখনও পাপ করছ?’ ভোগলোলুপ ইউরোপকে ত্যাগের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার দরকার ছিল। শুধু কথায় তার মন ভিজত না। দৃষ্টান্ত তাকে মুগ্ধ করলে। আমার কিন্তু এ দৃশ্য ভালো লাগে না। কসাইয়ের দোকানে গোরু-ভেড়ার ধড় ঝুলছে, তার ঠিক সামনে গির্জার দেওয়ালে যিশুর শবমূর্তি ঝুলছে, এ যেন যিশুকে বিদ্রূপ করা। মনে হয় যেন ইউরোপের লোক পরস্পরকে যিশুর দোহাই দিতে চায় এইজন্যে যে, তাদের কারুর পক্ষে যিশুর আদর্শ অন্তরের দিক থেকে সত্য নয়, অথচ বাইরের দিক থেকে সে-আদর্শের প্রয়োজন আছে।
চোখে দেখতে জার্মান ও ইংরেজ একইরকম, ফরাসিও ভিন্ন নয়। ইউরোপের সব জায়গায় একই পোশাক, একই খানা, একই আদবকায়দা; সব জাতির বহিরঙ্গ একই। স্থান ও পাত্র ভেদে যেটুকু ব্যতিক্রম দেখা যায় সেটুকু ধর্তব্য নয়। জার্মানদের ধারণা তারা ভয়ানক কেজো মানুষ। তাই তারা মাথা মুড়ায়, plus fours কিংবা breeches পরে সাধারণত। তাদের মেয়েদেরও মোটা কাপড়ের প্রতি টান—খদ্দরপরা মেয়ে অহরহ দেখছি। জার্মান মেয়েরা কায়িক শ্রমসাধ্য কাজে পুরুষের দোসর। তারা গোরু-ঘোড়ার গাড়ি হাঁকায় ও পিঠে বোঝা বেঁধে হাঁটে। ফরাসি মেয়েদের দেখলে যেমন মনে হয় সারাক্ষণ পুষিমেনির মতো শরীরটিকে ঘষে-মেজে সাজিয়ে রেখেছে, জার্মান মেয়েদের দেখলে তেমন মনে হয় না। আবার ইংরেজ পুরুষদের দেখলে যেমন মনে হয় মাথার চুল থেকে পায়ের জুতো অবধি ফিটফাট, জার্মান পুরুষদের দেখলে তেমন মনে হয় না। জার্মানরা কেজো মানুষ, স্মার্ট হওয়ার মতো শৌখিনতা তাদের সাজে না; সাজসজ্জায় তারা ভোলানাথ। তালি-দেওয়া চামড়ার হাফপ্যান্ট পরে পা দেখিয়ে রাস্তায় বার হলে লণ্ডনে ভিড় জমে যেত, মিউনিখে কেউ কিছু ভাবে না।
১৩
অস্ট্রিয়ায় যাওয়ার আগে বড়ো ভাবনা ছিল কী আর দেখব! গত মহাযুদ্ধে অস্ট্রিয়ায় যে-সর্বনাশ ঘটে গেল, কোন দেশের তেমন ঘটেছে! কত শতাব্দীর কত বড়ো সাম্রাজ্য, চারটি বছরের যুদ্ধে তার চৌচির অবস্থা! কোথায় গেল হাঙ্গেরি, কোথায় ট্রানসিলভানিয়া, কোথায় গেল ক্রাকাউ, কোথায় বোহেমিয়া, কোথায় গেল ক্রোয়েশিয়া, ড্যালমেশিয়া, বসনিয়া। চারটি বছরে চার শত বছরের কীর্তি নিঃশব্দে ভেঙে পড়ল, যেন একটা তাসের কেল্লা—একটি আঙুলের একটু ছোঁয়া সইতে পারলে না। সাম্রাজ্য যদিও চার শতাব্দীর, রাজবংশ প্রায় আট শতাব্দীর। যেন আলাউদ্দিন খিলজি থেকে পঞ্চম জর্জ পর্যন্ত একটি রাজবংশ দিল্লির সিংহাসনে বসে রাজ্যবিস্তার করে আসছিলেন, ভেবেছিলেন চন্দ্র-সূর্য যতদিনের তাঁরাও ততদিনের। ভালোই হল যে সাম্রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে সম্রাটও গেলেন, নইলে এখনকার ওইটুকু অস্ট্রিয়ায় অত বড়ো বনেদি রাজবংশকে মানাত না।
বড়ো ভাবনা ছিল ভিয়েনায় গিয়ে কী আর দেখব; সুন্দরী ভিয়েনার বিধবার সাজ কি আমার ভালো লাগবে! ভিয়েনাকে রানির বেশে সাজাবার সামর্থ্য অস্ট্রিয়ার নেই, অস্ট্রিয়ার না-আছে বন্দর, না-আছে খনি, অস্ট্রিয়ার লোকসংখ্যা এখন এত অল্প যে ভিয়েনার মতো বৃহৎ নগরীর নাগরিক হওয়ার জন্যে আমেরিকানদের সাধাসাধি করতে হয়। আর কিছুদিন পরে ভিয়েনাটাকেও তারা প্যারিস করে ছাড়বে—প্যারিসেরই মতো আমেরিকান উপনিবেশ।
ভিয়েনার সঙ্গে তার আশপাশের সংগতি নেই। একটা কৃষিপ্রধান দেশের এক প্রান্তে এত বড়ো একটা শিল্পপ্রধান শহর, যার ত্রিসীমানায় বন্দর বা খনি নেই। বন্দর যদি-বা ছিল অনেক দূরে, তাও কেড়ে নিয়েছে ইটালি। আর খনি যদি-বা ছিল অনেক দূরে, তাও পড়ল চেকোশ্লোভাকিয়ার ভাগে। কেবল টুরিস্ট নিয়ে তো একটা বড়ো শহর বাঁচতে পারে না। ভিয়েনার লোকসংখ্যা কমেছে। বাদশাহি জাঁকজমক আর নেই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ভিয়েনা অতুলনীয় সুন্দরী। তার প্রায় চারদিকে পাহাড়, কাছেই ড্যানিউব নদী, ভিতরে নদীর খাল। ‘Ring’ নামক রাজপথটি ভিয়েনারই বিশেষত্ব। বার্লিন দেখিনি, কিন্তু লণ্ডন-প্যারিসের চেয়েও ভিয়েনা দুটি কারণে সুন্দর। প্রথমত, ভিয়েনার পথঘাট প্যারিসের চেয়ে তো নিশ্চয়ই—লণ্ডনের চেয়েও পরিষ্কার। দ্বিতীয়ত, ভিয়েনার সৌধগুলি লণ্ডনের চেয়ে তো নিশ্চয়ই—প্যারিসের চেয়েও সুধা-ধবল। ধোঁয়া আর ফগের ভয়েই বোধ হয় লণ্ডনের বাড়িগুলো চুন মাখতে চায় না। কিন্তু আকাশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাটিও যদি অন্ধকার হয় তো মনের ওপরে তার প্রতিক্রিয়া হয় সাংঘাতিক। ভিয়েনায় এ আপদ নেই, তাই সেখানে নয়ন দুটি মেলিলে পরে পরান হয় খুশি।
কিন্তু ভিয়েনার নির্জনতা লণ্ডন-প্যারিসের মনকে ঘুম পাড়াতে চায়। মধ্যাহ্নকে মনে হয় মাঝরাত। কত বড়ো বড়ো বাড়ি, কত বড়ো বড়ো রাস্তা—কিন্তু এত জনবিরল যে ঘুমন্তপুরীর মতো লাগে। বৃহৎ রেস্তরাঁ, ঢুকে দেখা গেল লোক নেই, অথচ অমন রান্না সারা ইউরোপ ঢুঁড়লেও পাওয়া যায় না, অপিচ অত সস্তায়। প্যারিসে লোক কিলবিল করছে, মানুষ যত নেই মোটর আছে তত; আর সেসব মোটর যারা হাঁকায় তারা বিদ্যুতের সঙ্গে টক্কর দেবার স্পর্ধা রাখে। প্যারিস থেকে ভিয়েনায় গেলে বড়ো নিঃসঙ্গ বোধ হয়। অথচ ভিয়েনা চিরদিন এমন ছিল না। এই বিগতযৌবনা রূপসি একদিন ইউরোপের রানি ছিল। তখন কত ডিপ্লোম্যাট, কত বণিক, কত গুণী ও কত পর্যটক সোনা দিয়ে তার মুখ দেখতে আসত। সংগীতে ভিয়েনার সমান ছিল না। ভিয়েনার অপেরা এখনও তার পূর্বগৌরব হারায়নি। কিন্তু মহাকাব্যের মতো অপেরারও দিন যায় যায়। এমনই আমাদের দুর্ভাগ্য যে শিকাগোর অপেরা লণ্ডনে বসে দেখবার শোনবার উপায় হয়েছে ও হচ্ছে কিন্তু নতুন একখানা অপেরা লেখবার মতো প্রতিভা একমাত্র Strauss-এর আছে এবং সম্ভবত তাঁর সঙ্গেই লোপ পাবে। থিয়েটারে সাজসজ্জার যে উন্নতি হয়েছে তা শেক্সপিয়ারের পক্ষে কল্পনাতীত, কিন্তু শেক্সপিয়ারের পায়ের ধুলো নেবার উপযুক্ত নাট্যকার একটিও জন্মাচ্ছে না। এবং রবীন্দ্রনাথই বোধ হয় জগতের শেষ মহাকবি।
ঠাট বজায় রাখতে ভিয়েনার লোক অদ্বিতীয়। অত বড়ো সাম্রাজ্য হারাবার পরে সোশ্যালিস্ট হওয়া সত্ত্বেও তারা আগের মতোই কায়দাদুরস্ত আছে। রেস্তরাঁয় লোকই আসে না, তবু ওয়েটার বাবাজিদের দরবারি পোশাকটি অপরিহার্য। পাহারাওয়ালা অন্য সব দেশে কেবল পাহারাই দেয়, তার হাতে একটা বেটন থাকলেই যথেষ্ট, কিন্তু ভিয়েনার পাহারাওয়ালার গায়ে সৈনিকের সাজ ও কোমরে সুখচিত তরবারি। ভিয়েনার লোক কিছুতেই ভুলতে পারছে না যে তাদের সম্রাট ও তাঁর সভাসদেরা ছিলেন ইউরোপের মধ্যে অভিজাততম, যদিও এখন তারা ইউরোপের দরিদ্রতম জাতি বললে হয় এবং খেতে পায় না বলে লিগ অব নেশনসের মধ্যস্থতায় টাকা ধার নিয়েছে। অস্ট্রিয়াকে সম্ভবত একদিন বাধ্য হয়ে জার্মানির অন্তর্গত হতেই হবে, কিন্তু ভিয়েনা কেমন করে ভুলবে যে সে-ই ছিল জার্মানির তথা ইউরোপের দীর্ঘকালের রাজধানী! সেদিনকার বার্লিনের কাছে ভিয়েনা কেমন করে হাতজোড় করে দাঁড়াবে! যে-প্রাশিয়া একদিন তার ভৃত্যের মতো ছিল তার কাছে অস্ট্রিয়া হবে ছোটো! কিন্তু গরজ বড়ো বালাই। কত বড়ো বড়ো উঁচু মাথাকে সে ধুলোয় মিশিয়েছে। যে-কারণে এখন ছোটো ছোটো কারবার টিকতে পারছে না, পৃথিবীব্যাপী combine গড়ে উঠছে, ঠিক সেই কারণে এখন ছোটো ছোটো রাষ্ট্র টিকতে পারবে না, মহাদেশব্যাপী মহারাষ্ট্র গড়ে তুলতেই হবে।
অস্ট্রিয়ানদের দরিদ্র বললুম বলে যেন না মনে করেন ওরা আমাদের মতো দরিদ্র। ভিয়েনার পশ্চিম দিকে যাকে দারিদ্র্য বলা হয়, ভিয়েনার পূর্ব দিকে তার নাম সচ্ছলতা। অর্থাৎ ইউরোপের দরিদ্ররা এশিয়ার মধ্যবিত্ত। ইংল্যাণ্ডে যাকে slum বলে সেটা আমাদের উত্তর কলকাতার চেয়ে কুৎসিত নয়। ইউরোপের পারিয়াদের দাবির ফিরিস্তি আমাদের মধ্যবিত্তদের তাক লাগিয়ে দেয়—চড়া হারের মজুরি, বিনা পয়সায় চিকিৎসা, সস্তায় আমোদ-প্রমোদের টিকিট, ঘন ঘন ছুটি, প্রচুর পেনশন, আপদে-বিপদে জীবনবিমা। আরও কত কী! জীবনের কাছে আমাদের দাবি কোনোমতে বংশরক্ষা করা ও মরে গেলে পিন্ডিটুকু পাওয়া। এদের দাবি হয় রাজসিক জীবন নয় রাজসিক মৃত্যু। সামান্য কারণে এরা বিদ্রোহ করে বসে, যত সহজে মরে তত সহজে মারে। জীবনের মূল্য যত, প্রাণের মূল্য তত নয়। স্বল্পতম ভার সইতে পারে না বলে এদের সমাজ লোকসংখ্যা বাড়লেই যুদ্ধের অছিলা খোঁজে। এদের সমাজকে পাতাবাহারের গাছের মতো মাঝে মাঝে ছাঁটলে তবে তার স্বাস্থ্য থাকে। নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের আদর্শটি এদের কাছে এত মূল্যবান যে, এইজন্যে যুদ্ধের আর বিরাম নেই। এইজন্যে এরা পিন্ডাধিকারী না রেখে চিরকুমার অবস্থায় মরাটাকে অধর্ম জ্ঞান করে না, বেশি বয়সে বিয়ে করার আনুষঙ্গিক অন্যায়—হয় আত্মনিগ্রহ নয় অপকীর্তি—তো করেই, বিয়ের পরেও যেকোনো মতে জন্মশাসন করে। এত বড়ো ইউরোপে কোথাও একটি পশু-পাখি-সাপ-ব্যাং-মশা-মাছি দেখতে পাওয়া শক্ত, অন্নের ভাগ দিতে পারবে না বলে অভক্ষ্য প্রাণীকে এরা মেরে সাবাড় করেছে ও ভক্ষ্য প্রাণীকে অন্নে পরিণত করেছে। একটা পোষা প্রাণীর যদি স্বাস্থ্য গেল তো তাকে এরা তখুনি গুলি করে ভাবলে দু-পক্ষের আপদ চুকল। অপরপক্ষে কিন্তু পোষা প্রাণীকে এরা রুগণ হতেই দেয় না, এত যত্নে রাখে। পীড়িত পশুকে দিয়ে গাড়ি টানালে কঠিন সাজা। হত্যা ব্যাপারটা যাতে এক মুহূর্তে সমাপ্ত হয়, পশুর পক্ষে যন্ত্রণাকর না-হয়, সেজন্যে কসাইদের পিস্তল ব্যবহার করতে বাধ্য করা হচ্ছে। একটা মুমূর্ষু প্রাণী দশ দিন ধরে—না দশ ঘণ্টা ধরে—একটু একটু করে মরছে ও অসহ্য যন্ত্রণা পাচ্ছে এ দৃশ্য ইউরোপে দেখবার জো নেই। নিজে যন্ত্রণা পেতে ভালোবাসে না বলে এরা যন্ত্রণা দিতে ভালোবাসে না। Vivisection-এর বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চলছে। ইউরোপের সব দেশেই এখন নিরামিষাশী সংখ্যা বাড়ছে এবং প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ হয়েছে অনেকেই।
অনাবশ্যককে ইউরোপ নির্মমভাবে ছেঁটেছে। বুড়ো-বুড়িকেও না খাটিয়ে খেতে দেয় না। ‘Dying in harness’ তার জীবনের আদর্শ। সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যকের বহরকেও সে বাড়াতে লেগেছে। যৌবন আগে ছিল গোটা কয়েক বছরের। এখন চাই শতবর্ষের যৌবন। এরজন্যে কত প্রাণী হত্যা করতে হবে, কত মানুষকে যুদ্ধে মারতে হবে, কত লোককে আর্থিক প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করতে হবে, কত অজাত শিশুকে জন্মাতে দেওয়া যাবে না, কত শিশুকে প্রকারান্তরে হত্যা করতে হবে। এত কান্ড করলে তবে হবে জন কয়েকের দীর্ঘ যৌবন, নিখুঁত স্বাচ্ছন্দ্য। দুর্ভিক্ষের চেয়ে, আত্মনিগ্রহের চেয়ে, শিশুমৃত্যুর চেয়ে, চির রুগণতার চেয়ে এ ভালো না মন্দ?
দূর থেকে শুনতুম অস্ট্রিয়ানদের মরো-মরো অবস্থা, তারা বুঝি আর বাঁচে না! দেখলুম তারা দিব্যি আছে, আমাদের চেয়ে সচ্ছলভাবে। বুঝলুম ইউরোপের লোক সামান্য অসুবিধাকেও বাড়িয়ে দেখে, চার বেলার এক বেলা না খেতে পেলে বলে, দুর্ভিক্ষে মরে গেলুম। লণ্ডনে সেদিন দশ-বারোটা লোক নাকি অনশনে মরেছিল, তাই নিয়ে মন্ত্রীমন্ডলীর আসন টলে উঠল। অথচ ওরা যদি যুদ্ধে মরত তবে কেউ ওদের কথা ভুলেও ভাবত না। ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকদের দুর্ভাবনা এই যে তাদের স্ত্রীরা পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে অনবদ্য স্বাস্থ্য অটুট রাখতে পারে না, তাদের স্বামীদের মজুরি এত কম! আর আমাদের বড়োলোকের মেয়েরাও কুড়িতে বুড়ি হন। দূর থেকে আমাদের দেশটাকে মাঝে মাঝে মনে হয় একটা বিরাট Slow suicide club—এত আমাদের সহিষ্ণুতা, অল্পে সন্তোষ, আত্মনিগ্রহ, চক্ষুলজ্জা। আমরা বলি, নিজের ছাড়া বাকি সকলের উপকার করো। এরা বলে, ‘Help yourself’, কেননা ‘God helps those who help themselves’, অর্থাৎ নিজের মাথায় যদি তেল ঢালো তো ভগবান তোমার তেলা মাথায় তেল ঢালবেন। বেকারসমস্যা নিয়ে ইংল্যাণ্ড বড়ো বিব্রত। অথচ ইংল্যাণ্ডের ধনীরা যদি একখানা করে রুটি দেয় তবে ইংল্যাণ্ডের যত বেকার আছে প্রত্যেকেই এক-একজন মোহান্ত মহারাজের মতো বৈষ্ণবী নিয়ে পরম আহ্লাদে মালা জপতে পারে। শুধু তাই নয়, ইংল্যাণ্ডের ধনীরা ইচ্ছা করলেই বিশ-ত্রিশ কোটি ইঁদুর বাঁদর প্রভৃতি কেষ্টর জীবের জন্য একটা দেশব্যাপী চিড়িয়াখানাও স্থাপন করতে পারে। কিন্তু ভিক্ষা দিয়ে অপরের উপকার করা এদেশের প্রকৃতিবিরুদ্ধ—যোগ্যতা না দেখলে, বাধ্য না-হলে কেউ দেয় না। ধনী-দরিদ্রের মধ্যে এমন মনকষাকষি আমাদের দেশে নেই, এত দলাদলিও আমাদের দেশে নেই। তবে সন্ধি করবার কায়দাও এরা জানে। সময় বুঝে সন্ধি না করলে দু-পক্ষের একপক্ষ অবশিষ্ট থাকবে না, এক হাতে তালি বাজবে না। যুদ্ধটা হচ্ছে সহিংস সহযোগ, ও-ব্যাপার একা একা হয় না। ভবিষ্যতে আবার লড়বে বলে শত্রুকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়, কেননা শত্রুই হচ্ছে যুদ্ধের সহযোগী। যে-জন্তুকে এরা শিকার করবে সে-জন্তুকেও এরা বনজঙ্গলে পালন করে। খাবার জন্যেই এরা গোরু শূকরকে খাইয়ে মোটা করে।
ইউরোপের বহিঃপ্রকৃতি তার অন্তঃপ্রকৃতিকে কী পরিমাণ নিষ্করুণ করেছে তার একটা নিদর্শন ইউরোপের যে-দেশে যাই সেদেশে দেখি। আমাদের যেমন চালের দোকান এদের তেমনি মাংসের দোকান; প্রায় প্রত্যেক গলিতে গলিতে আছেই, কষ্ট করে খুঁজতে হয় না, আপনি খোঁচা দেয়। বেচারা মুসলমানেরা ক-টাই বা গোরু খায়? যদি-বা খায় তবে ক-টা গোরুর ছাল ছাড়া ধড় রাস্তায় রাস্তায় দোকানে দোকানে সাজিয়ে ঝুলিয়ে রাখে? খদ্দের এলে করাত দিয়ে নির্দিষ্ট স্থানের মাংস কেটে ওজন করে প্যাক করে বিক্রি করে। একসঙ্গে একশোটা মরা পাখি পাকা কলার মতো ঝুলছে কিংবা একশোটা মরা খরগোশ। সাজিয়ে রাখাটাকে এরা একটা আর্ট করে তুলেছে বলে বীভৎস ঠেকে না, ক্রমে ক্রমে কলা-মুলো-কপি-কুমড়োর মতো লাগে, আমিষ-নিরামিষের পার্থক্যবোধ লোপ পায়। রাগ করবার উপায়ও নাই, কেননা মাছকেও তো আমরা কলা-মুলোর সামিল মনে করে থাকি, বিশেষ করে বাঙালির চোখে মাছ একটা প্রাণীই নয়। প্রাণ সম্বন্ধে ওই অসাড়তাটাকে আরেকটু প্রশ্রয় দিলে আমরাও ইউরোপীয় হয়ে পড়তুম, ঝুলন্ত হ্যাম দেখে—চোখে নয়—জিভে জল এসে পড়ত।
দোকান সাজানোতে ইংরেজ-জার্মান-অস্ট্রিয়ান-সুইসরা ওস্তাদ। ফরাসিরা আমাদের মতো এলোমেলো! শুধু দোকান নয়, রেল স্টিমার হোটেল রেস্তরাঁ পথঘাট প্রদর্শনী সর্বত্র একটি শৃঙ্খলা ও পারিপাট্য উত্তর ইউরোপের বিশেষত্ব বলেই মনে হয়। ভিয়েনা ও প্যারিস এই দুটি শহরের মধ্যে ভিয়েনা অনেক বেশি সৌষ্ঠবসম্পন্ন, যদিও এলোথেলো সৌন্দর্য প্যারিসেরই বেশি। ভিয়েনায় তো সেন নদীর মতো আঁকাবাঁকা নদী নেই, তার কূলে বসে মাছধরা নেই, তার কূলে দাঁড়িয়ে ছবি আঁকা নেই, তার বাঁধে পুরোনো বইয়ের দোকানে ঝুঁকেপড়া বইপাগলা বুড়ো নেই, তার আশেপাশের রাস্তায় রঙিন কার্পেট কাঁধে নিয়ে পায়চারি করতে থাকা ইজিপশিয়ান ফেরিওয়ালা নেই। এতরকম রাস্তার দৃশ্য (street sights) প্যারিসের মতো আর কোথায় আছে? সারাক্ষণ যেন অভিনয় চলছে প্রতি রাস্তায়। অথচ নোংরা রাস্তা, মোড়ে জল জমেছে, ফুটপাথে দোকানের নীচে দোকান, তাতে একসঙ্গে একশোরকম জিনিস জট পাকিয়েছে, তরমুজ আর বাঁধাকপির সঙ্গে খরগোশ আর মাছ এবং গেঞ্জি আর পুলোভার। দোকানের গায়ে গায়ে একটা কাফে আর মদের দোকান—সেও অকথ্য নোংরা অগোছালো। এসব অনাচার ভিয়েনায় কিংবা লণ্ডনে নেই, কোলোনে কিংবা মিউনিখে নেই, বার্নে কিংবা লুসার্নে নেই। মার্সেলসে আছে, ভার্সেলসে আছে এবং সম্ভবত সমস্ত ফ্রান্সে আছে। এবং সম্ভবত সমস্ত দক্ষিণ ইউরোপে। প্রদীপের নীচে অন্ধকারের মতো ফরাসিদের নিখুঁত বাস্তুকলার সঙ্গে প্রচুর ধুলো কাদা যোগ দিয়েছে। ভিয়েনা চিত্রে-ভাস্কর্যে-বাস্তুকলায় প্যারিসের নকল, কিন্তু শৃঙ্খলায় ও পারিপাট্যে প্যারিসের বাড়া। অবস্থা বিপর্যয় সত্ত্বেও তার এই গুণগুলি যায়নি, তার সোশ্যালিস্ট মিউনিসিপ্যালিটির মেজাজটা বোধ হয় বাদশাহি।
বাদশাহের প্রাসাদগুলি অবশ্য এখন মিউজিয়ামে পরিণত হয়েছে। দশ বছর আগে যে-বাগানে বাদশাজাদিরা হাওয়া খেতেন এখন সেখানে গরিবের মেয়েরা খেলা করতে যায়। দশ বছর আগে যেসব ঘরে বাদশাহ শয়ন, বিশ্রাম, ভোজন করতেন, যেসব ঘরে বেগম সখীদের সঙ্গে গল্প করতেন বা অতিথিচর্চা করতেন, বা নাচের মজলিশ ডাকতেন, সেসব ঘর এখন সামান্য কিছু দর্শনি দিলে কিছুক্ষণের জন্য রাস্তার লোকের সম্পত্তি। দশ বছর আগে সাধারণের চোখে যা আলাদিনের প্রদীপের মতো ছিল তাই এখন ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে। সাধারণ মানুষ তারই মতো সাধারণ মানুষকে বাদশাহ পদবি দিয়ে তারই গৃহের মতো সাধারণ গৃহকে অমরাবতী কল্পনা করেছিল এবং সমস্ত ব্যাপারটির গায়ে পুরাণ ইতিহাসে রূপকথার সোনার কাঠি ছুঁইয়ে সেটিকে নিজের প্রতিদিনের জীবন থেকে লক্ষ যোজন দূরে রেখেছিল। ঈশ্বরভক্তির মতো রাজভক্তিও মানুষের নিজের তৃপ্তির জন্য; এবং একটা কাল্পনিক দূরত্বই তার প্রাণ। আজ সে-দূরত্ব ঘুচে গেছে; প্রকাশ হয়ে পড়েছে যে রাজপ্রাসাদটা বাহির থেকে হাঁ করে দেখবার মতো এমন কিছু মায়াপুরী নয়, বারো আনা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলে নিতান্তই রক্ত-মাংসের মানুষের আহার-নিদ্রার স্থান এবং ছোটো ছোটো মান-অভিমান পরশ্রীকাতরতার দাগে দাগি। মানুষে মানুষে যে কাল্পনিক ব্যবধান এতকাল এত কাব্য ও এত কলহ উদ্রেক করেছিল, আজ মনে হচ্ছে সব মিথ্যা, সব স্বপ্ন। এবার মানুষ যে নতুন জগতের দ্বারে দাঁড়িয়েছে সে-জগৎ দিনের আলোর জগৎ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বারা তার নাড়িনক্ষত্র জানা, কোথাও একটু কল্পনার অবকাশ নেই, নিদারুণ মোহভঙ্গের মধ্যে তার পথ। কোন রাজপ্রাসাদকে দেখে স্বর্গ কল্পনা করবে? কোন রাজাকে দেখে দেবতা? কোন রাজপুত্রকে নিয়ে উপকথা রচনা করবে? কোন রাজবংশকে নিয়ে কাব্য? তাই শেক্সপিয়ারও আর হয় না, রবীন্দ্রনাথও আর হবে না।
১৪
যতগুলো রাজপ্রাসাদ দেখলুম তাদের কোনোটাই মনে ধরল না, কেননা কোনোটাই যথেষ্ট আড়ম্বরপূর্ণ নয়। পোশাকে প্রাসাদে যানে-বাহনে বেগমে-গোলামে আমাদের রাজরাজড়ারাই দুনিয়ার সেরা। আগ্রা, দিল্লি, লখনউ, বেনারসের সঙ্গে ভার্সেলস, ভিয়েনা, মিউনিখ বুডাপেস্টের এইখানেই হার যে রাজাতে-প্রজাতে ভারতবর্ষে যেমন আসমান-জমিন ফরক সম্ভবত এক রাশিয়া ছাড়া ইউরোপের আর কোথাও তেমন ছিল না। আমরা ধাতে এক্সট্রিমিস্ট। আমরা রাজা-বাদশা ও ভিখারি ফকির ছাড়া কারুকে সম্মান করিনে। তাই আমাদের দেশে ভোগের নামে লোকে মূর্ছা যায়, ভাবে না-জানি কোন রাজারাজড়ার মতো ভোগ করতে গিয়ে ভিখারিতে সমাজ ভরিয়ে দেবে। আর ত্যাগের নাম করলে ধড়ে প্রাণ আসে—হ্যাঁ, সমাজের পাঁচজনের ওপরে লোকটার দরদ আছে বটে। দেখছ না আমাদেরই জন্যে উনি কৌপীন ধরলেন।
ভোগের আড়ম্বর ও ত্যাগের আড়ম্বর বোধ হয় কেবল ভারতবর্ষের নয়, প্রখর সূর্যালোকিত দেশগুলির দুর্ভাগ্য। ইজিপ্টে ও গ্রিসে সমাজের একটা ভাগ দাসত্ব করেছে, অপর ভাগ সেই দাসত্বের ওপরে পিরামিড খাড়া করেছে। অতটা এক্সট্রিমিজম প্রকৃতির সহ্য হয় না, ইজিপ্ট ও গ্রিস টলে পড়েছে। দাসও মরেছে, দাসের রাজাও। ভারতবর্ষেও কোনো একটা রাজবংশ দু-চার পুরুষের বেশি টেকেনি, যত বিজেতা এসেছে সবাই দু-চার পুরুষ পরে বিজিত হয়েছে। ইংরেজের বেলা এর ব্যতিক্রম হল, কেননা ইংরেজ ভারতবর্ষের জল-হাওয়া কিংবা ধাত কোনোটাকেই স্বীকার করেনি, ইংরেজ দূর থেকে শাসন করে এবং ঘরের প্রভাববশত মনেপ্রাণে নাতিশীতোষ্ণ থাকে। ইংরেজের temper গরমও নয়, নরমও নয়; অসহিষ্ণুও নয়, সহিষ্ণুও নয়। ইংরেজ আশ্চর্যরকম মধ্যপন্থী। তবে এও ঠিক যে ইংরেজ অত্যন্ত বেশি মাঝারি। এই মাঝারিত্বকে লোকে গালাগাল দিয়ে বলে conservatism; আসলে কিন্তু ইংরেজের conservatism স্থাণুত্ব নয়, ধীরে-সুস্থে চলা, slow but sure—কচ্ছপ-গতি। সূর্যের আলোর মদে মাতাল ফরাসিরা কতকটা আমাদেরই মতো এক্সট্রিমিস্ট, তাই তারা সুদীর্ঘকাল মহাশয়ের মতো যা-ই সওয়াবে তা-ই সয়, অবশেষে একদিন এটনা আগ্নেয়গিরির মতো অগ্নিবৃষ্টি করে আবার চুপচাপ বসে মদে চুমুক দেয়। তার ফলে খরগোশকে ছাড়িয়ে কচ্ছপ এগিয়ে যায়।
তবে ফরাসি বলো জার্মান বলো ইংরেজ বলো কেউ আমাদের মতো ছোটোতে-বড়োতে আসমান-জমিন ব্যবধান ঘটতে দেয় না, সময় থাকতে প্রতিকার করে। এই যে সোশ্যালিস্ট মুভমেন্ট এটার মতো মুভমেন্ট প্রতি শতাব্দীতে ইউরোপের প্রতি দেশে দেখা দিয়েছে। আজ যদি এ মুভমেন্ট অতি বৃহৎ হয়ে থাকে তবে যার বিরুদ্ধে এ মুভমেন্ট সেও আজ অতি বৃহৎ হয়ে উঠেছে। সমাজের একটা পা আজ বিপর্যয় লাফ দিয়ে এগিয়ে গেছে বলেই অপর পা-টা বিপর্যয় লাফ দিয়ে সঙ্গ রাখতে ব্যগ্র। ইউরোপের ধনীরা আজকের এই উন্মুক্ত পৃথিবী থেকে যে প্রচুর ধন আহরণ করে ঘরে আনছে ইউরোপের শ্রমিকরা সেই প্রচুর ধনেরই একটা সমানুপাত বণ্টন চায়।
এক হাজার বছর আগেও আমাদের দেশে বৈরাগ্যাভিমানী ছিল বিস্তর, এরা সমাজের সেই ভাগটা, যে-ভাগ বৃহৎ ব্যবধান সইতে না-পেরে সুতোছেঁড়া ঘুড়ির মতো আকাশে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। এরা ধনীলোকের ধনভার লাঘব করে দরিদ্রের দারিদ্র্যভার লাঘব করেনি, কেননা সেজন্যে অনেক দুঃখ ভুগতে হয় এবং কোনোদিন সে-ভোগের শেষ নেই। প্রকৃতির অনাদ্যন্ত এই যে সাধনা এই ভারসাম্যের সাধনায় প্রকৃতির সঙ্গে সন্ন্যাসী যোগ দেয় না, সে চিরকালের মতো সিদ্ধি চায়। যে-জগতে প্রতিদিন বড়ো বড়ো গ্রহ-নক্ষত্র ভাঙছে, মহাশূন্যের গর্ভে বড়ো বড়ো নৌকাডুবি ঘটছে, প্রতিদিন ছোটো ছোটো অণু-পরমাণু থেকে সব নব নব গ্রহ-নক্ষত্র গড়ে উঠছে, ছোটো ছোটো প্রবালকীট মিলে অপূর্ব প্রবালদ্বীপ গেঁথে তুলছে—এই প্রতিদিনের খেলাঘরে সন্ন্যাসীকে কেউ পাবে না। সে তার কাঁথা-কম্বল-ছাল-বল্কল আঁকড়ে ধরে বিবাগি হয়ে গেছে। এদিকে মহারাজের অন্তঃপুরে রানিমক্ষিকার সংখ্যা বাড়ছে এবং দাসমক্ষিকাদের ক্রন্দনগুঞ্জনে সংসারচক্র মুখর হল। প্রাসাদে আর কুটিরে ভারতবর্ষের মাটি আর মর্ত নয়, একাধারে স্বর্গ—পাতাল। আল্পস পর্বত ও ভূমধ্যসাগর সহ্য হয়, কেননা উঁচু-নীচু হলেও তাদের ব্যবধান দুরতিক্রম্য নয়, কিন্তু হিমালয় পর্বত ও ভারতসাগর সহ্য হয় না। উপরে ত্রিশ হাজার ফিট ও নীচে বিশ হাজার ফিট—পঞ্চাশ হাজার ফিটের ব্যবধান দুরতিক্রম্য। ভারতবর্ষের রাজা-মহারাজারা যে-চালে থাকেন ইউরোপের সম্রাটদের পক্ষেও তা স্বপ্ন এবং ভারতবর্ষের চাষি-মজুররা যে-চালে থাকে ইউরোপের ভিখারিদের পক্ষেও তা দুঃস্বপ্ন। এবং এই ব্যাপার খুবসম্ভব হাজার হাজার বছর থেকে চলে আসছে। কেননা আমরা চিরকাল Intemperate Zone-এর লোক। আর আমাদের দেশটাও চিরকাল এত বেশি উঁচু-নীচু যে আমাদের চোখে জীবনের বিশ্রীরকম উঁচু-নীচুও একটা সহজ উপমার মতো স্বাভাবিক ঠেকে।
রাজপ্রাসাদগুলি পরিদর্শন করবার সময় লক্ষ করেছি সেগুলি কেবল রাজপ্রাসাদ নয়, সেগুলির প্রত্যেকটি একটি পুরুষ ও একটি নারীর দুঃখ-সুখের নীড়—এক-একটি ‘home’। ইংরেজি home কথাটির ভারতীয় প্রতিশব্দ নেই, কেননা home কেবল গৃহ নয়, একটি নারীর ও একটি পুরুষের কাঠ-পাথরে রূপান্তরিত প্রেম। ইংরেজ যুবক যখন বিবাহ করে তখন তার স্ত্রী তার কাছে এমন একটি গুহা প্রত্যাশা করে যেখানে সে সিংহীর মতো স্বাধীন, যেখানে তার স্বামী পর্যন্ত তার অতিথি; শাশুড়ি, শ্বশুর, জা, দেবর তার পক্ষে ততখানি দূর, শাশুড়ি, শ্বশুর, শ্যালক, শ্যালিকা তার স্বামীর পক্ষে যতখানি। গুহার বাইরে তার স্বামীর এলাকা, গুহার ভিতরে তার নিজের; কেউ কারুর এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করতে পারে না। বাড়িতে একটা চাকর বহাল করবার অধিকারও স্বামীর নেই, কিংবা চাকরকে জবাব দেওয়ার। বাজার করাটাও স্ত্রীর এলাকা, কেবল দাম দেওয়ার বেলা স্বামীকে ডাক পড়ে। এক অফিসে এবং ক্লাবে ছাড়া স্বামীকে কেউ চেনে না, আসবাবের দোকানে, গহনার দোকানে, পোশাকের দোকানে, ধোপার বাড়িতে, ছেলে-মেয়েদের স্কুলে, বাড়িওয়ালার কাছে নিমন্ত্রণে-আমন্ত্রণে, পার্টিতে, নাচে, সর্বত্র স্ত্রীর বৈজয়ন্তী। এ সমস্তই home-এর এলাকায় পড়ে। অতএব home-কে আপনারা কেউ চারখানা দেওয়াল ও একখানা ছাদ ঠাওরাবেন না। ছেলের দোলনা থেকে ছেলের বাপের খাবার টেবিল পর্যন্ত যাঁর রানিত্ব নয় তিনি সুগৃহিণী নন, সমাজে তাঁর নিন্দা, তিনি কুনো। গির্জায়, charity bazaar-এ, সমাজসেবার সব আয়োজনে যাঁর হাত (বা হস্তক্ষেপ) তিনিই সুগৃহিণী।
এত যদি স্ত্রীর অধিকার তবে feminism-এর ঝড় উঠল কেন? কারণ industrial revolution-এর ফলে সমাজে একটা ভূমিকম্প ঘটে গেছে, ছেলেরা সারাজীবন দেশ-দেশান্তরে ঘুরছে, মেয়েরা home করবে কাকে নিয়ে? Home-এর মধ্যে একটা স্থায়িত্বের ভাব আছে, স্থানিক স্থায়িত্ব না হোক, সাময়িক স্থায়িত্ব। প্রেম স্থায়ী না হলে home হয় না। স্বামী-স্ত্রী ঠাঁই ঠাঁই হলেও ভাবনা ছিল না, দুজনের হৃদয়ও যে ঠাঁই ঠাঁই হতে আরম্ভ করেছে। আমরা হলে বলতুম দুয়ো-সুয়ো চলুক-না? অন্তত সদর মফসসল? মুশকিল এই যে, এতটা পতিব্রতা হতে এদেশের মেয়েরা এখনও শিখল না। সুয়োকে কোথায় বোন বলে আপনার করে নেবে ও স্বামীর শয্যায় পাঠিয়ে দেবার পার্ট প্লে করবে—আরে ছি ছি, রাম রাম, স্বামীদেবতাকে বিগ্যামির অপরাধে পুলিশে দেয়! আর মফস্সলের খবর পেলে একেবারে ডিভোর্স কোর্ট—ধিক! এরই নাম সভ্যতা!
ইংরেজ, জার্মান, স্কান্ডিনেভিয়ান মেয়েরা নিজের পাওনাগন্ডাটি চিরকাল বুঝে নিয়েছে। অতীত কালে এরা স্বামীকে বলেছে তোমাকেই আমি চিনি, তোমার মা-বাবাকে না। তাই এদের স্বামীরা পিতৃপিতামহের সনাতন ট্রাইব ছেড়ে স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে ফ্যামিলি সৃষ্টি করেছে। ফ্যামিলি ও পরিবার এককথা নয়, যেমন home ও গৃহ এককথা নয়। এ মজ্জাগত পাওনাগন্ডা বুঝে নেওয়ার স্বভাব থেকেই বর্তমান কালে feminism-এর উৎপত্তি। এর মূল সুরটি এই যে, home-এর দায়িত্ব যখন তোমরা স্বীকার করছ না তখন আমরাও স্বীকার করব না, তোমরা মুক্ত হও তো আমরাও মুক্ত হই। আপনারা বলবেন, সহিষ্ণুতাই নারীর ধর্ম, মা বসুমতী কত সইছেন! কিন্তু ম্লেচ্ছ মেয়েরা এত বড়ো তত্ত্বকথাটা বোঝে না, তাই তাদের স্বামীদের পদভারে মা বসুমতী টলমল এবং তাদের পদভারে তাদের স্বামীরা শিবের মতো চিতপাত।
ভিয়েনার রাজপ্রাসাদগুলিতে রানি মারিয়া থেরেসার ব্যক্তিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। রানি বলতে অসপত্ন রানি বুঝতে হবে—জা-শাশুড়িহীন, এবং সামাজিক প্রাণী। দিল্লি, আগ্রা, ফতেপুর সিক্রিতে বেগমের ব্যক্তিত্বের চিহ্ন-বিশেষ যদি-বা দেখা যায় তবু ওসব রাজপ্রাসাদকে home মনে করতে পারিনে। এবং সামাজিক প্রাণী হিসেবে বেগমের অস্তিত্ব ছিল না। সমাজের পাঁচজন পুরুষ তাঁদের চোখে দেখেননি, তাঁদের আতিথ্য পাননি; রাজন্যশ্রেণির পাঁচজন পুরুষ তাঁদের সঙ্গে দু-দন্ড আলাপ করতে পারেননি, দু-দন্ড নাচবার আস্পর্ধা রাখেননি। বাঁদি ও বান্দায় ভরা বিশাল বেগমমহলে বাদশা মাসে এক বার পূর্ণচন্দ্রের মতো উদয় হন, পুত্র-কন্যারা মা-বাবার সঙ্গে দু-বেলা আহার করবার সৌভাগ্য না পেয়ে দাস-দাসীর প্রভাবে বাড়েন। এমন গৃহকে গৃহিণীর সৃষ্টি বলতে প্রবৃত্তি হয় না। তাই প্রাচ্য রাজপ্রাসাদ আড়ম্বরে অপ্সরাপুরীর মতো হয়েও দুঃখে-সুখে নীড়ের মতো নয়। এখানে বলে রাখা ভালো যে লুই রাজার বা নেপোলিয়নেরও মফসসল ছিল, কিন্তু সেটা নিপাতন ও সমাজের স্বীকৃতি পায়নি। বস্তুত প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে রাজার সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ এক নয়। আমাদের রাজারা সমাজের আইনকানুনের উপরে; তাঁরা সমাজহীন। এদের রাজারা সামাজিক মানুষ, কিছুদিন আগে পর্যন্ত পোপের নির্দেশ অনুসারে রাজা ও প্রজা উভয়েই চালিত হত। ইংল্যাণ্ডের রাজা চার্চ অব ইংল্যাণ্ড ও পার্লামেন্টের কাছে এতটা দায়ী যে তাঁর বিবাহ ও বিবাহচ্ছেদ পর্যন্ত সমাজের এই দুটি হাতে। রাশিয়ার অত বড়ো স্বেচ্ছাচারী জারও স্ত্রী বিদ্যমানে পুনর্বার বিবাহ করতে পারতেন না কিংবা সুয়োরানির ছেলেকে রাজ্যাধিকার দিয়ে যেতে পারতেন না। সেক্ষেত্রে তিনি গ্রিক চার্চের নির্দেশ-সাপেক্ষ। তবে এও অস্বীকার করছিনে যে, পোপ বা প্যাট্রিয়ার্করা মাঝে মাঝে ঘুস খেয়ে ছাড়পত্র লিখে দিতেন। কিন্তু সেটা নিপাতন ও তার বিরুদ্ধে সমাজের বিবেক চিরদিন বিদ্রোহ করেছে। প্রোটেস্টান্টিজম তো এই জাতীয় একটা বিদ্রোহ! ওটাও আধুনিক সোশ্যালিস্ট মুভমেন্ট বা এর আগের গণতান্ত্রিক আন্দোলনেরই মতো মানুষে মানুষে দুরতিক্রম ব্যবধানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।
আসবাব-শিল্পের জন্যে ভিয়েনার খ্যাতি আছে। এই মুহূর্তে ইউরোপের সর্বত্র আসবাব-শিল্পের বিপ্লব চলেছে। কোলোনে, মিউনিখে ও ভিয়েনায় নতুন ধরনের ঘর ও নতুন ধরনের আসবাবের কতরকম নমুনা দেখা গেল। গত মহাযুদ্ধের পর ইউরোপের অধিকাংশ দেশেই এখন দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের মাঝখানের আর্থিক ব্যবধান ঘুচে গেছে। চাষি-মজুরদের অবস্থার যতটা উন্নতি হয়েছে মধ্যবিত্তদের অবস্থার ততটা উন্নতি হয়নি। কাজেই দুই শ্রেণির জন্যে অল্প দামের মধ্যে মজবুত অথচ বৈশিষ্ট্যসূচক বাড়ি ও আসবাব দরকার হয়েছে লাখে লাখে। যার যে-নমুনা পছন্দ হয় সে অবিলম্বে সেরকম জিনিসটি পায়। Large scale production-এর নীতি অনুসারে খরচ বেশি পড়ে না, হাঙ্গামাও নেই, পছন্দ করবার পক্ষে নমুনাও যথেষ্ট। মনে রাখতে হবে যে, ঘরের সাইজ ও রং ইত্যাদি অনুসারে আসবাবের সাইজ, রং, রেখা ও গড়ন। দুই দিকেই বিপ্লব ঘটেছে—বাড়ি ও আসবাব দুই দিকের দুই বিপ্লব পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেছে। দুই-ই সরল, লঘুভার, নাতিবৃহৎ, বাতালোকপূর্ণ, বিরলবসতি, নিরলংকার। মানুষের রুচি এখন সভ্যতার অতিবৃদ্ধিকে ছেড়ে প্রকৃতির উদার উন্মুক্ত বলকারক সত্যগুলির দ্বারস্থ হয়েছে। সেইজন্যে নতুন ধরনের চেয়ার, টেবিল, খাট বা দেরাজের উপরে পাগলামির ছাপ যদি-বা দেখতে পাওয়া যায়, চালাকির মারপ্যাঁচ বা বড়োমানুষির চোখে-আঙুল-দেওয়া ভাব একরকম অদৃশ্য। এর একটা কারণ, আগে যে-শ্রেণির লোক slum-এ থাকত তাদেরও চাহিদা অনুসারে এসবের জোগান এবং তাদের রুচি অতি সূক্ষ্ম ও অতি খুঁতখুঁতে নয় বলে তাদের সঙ্গে তাদের নামমাত্র উপরিতন মধ্যবিত্ত শ্রেণিকেও রুচি মেলাতে হচ্ছে। Mass production-এর মজা এই যে, চাষি-মজুরের সিকিটা-দুয়ানিটার জন্যে যে সিনেমার ফিলম, তার রুচির সঙ্গে কলেজের ছাত্রের রুচি না মেলে তো কলেজের ছাত্র নাচার। সিকি-দুয়ানির দিক থেকে কলেজের ছাত্র ও চাষি-মজুর দু-পক্ষই সমস্কন্ধ, অগত্যা রুচির দিক থেকেও দু-পক্ষকে সাম্যবাদী হতে হবে।
১৫
ইংল্যাণ্ড দেশটা যে কী সাংঘাতিক ছোটো, একটু ঘুরে-ফিরে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। ছোটো তো আমাদের এক-একটা প্রদেশও, কিন্তু তাদের ছোটোত্ব মানুষের হাতে-গড়া। আর ইংল্যাণ্ডের ছোটোত্ব নৈসর্গিক। এর সর্বাঙ্গ ঘিরেছে আঁটো পোশাকের মতো সমুদ্র, এর মাথার উপরে চাপ দিয়েছে টুপির মতো আকাশ। আকাশ? না, আকাশ বলতে আমরা যা বুঝি তা এদেশে নেই। সেইজন্যেই তো দেশটাকে অস্বাভাবিক ছোটো বোধ হয়—একটা অন্ধকূপ বিশেষ। এর ভিতরে যারা থাকে তারা পরস্পরের বড্ড কাছাকাছি থাকে, পরস্পরের নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পায়, হৃৎপিন্ডের স্পন্দন গোনে। ইংল্যাণ্ডে যখনই যে এসেছে সে বেমালুম ইংরেজ হয়ে গেছে। এর উদরের জারক রস এতই প্রবল যে আমিষ ও নিরামিষ, দুধ ও তামাক যখন যাই পেয়েছে তখন তা-ই পরিপাক করে এক রক্ত-মাংসে পরিণত করেছে। ইংল্যাণ্ডের আশ্চর্য একতার কারণ ইংল্যাণ্ড দেশটা দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ও উচ্চতায় অত্যন্ত আঁটোসাটো ও ছোটো।
ভারতবর্ষে যখন সারাদিনের খাটুনির শেষে তারা-ভরা আকাশের তলে বসে নিশ্বাস ছাড়ি তখন সে-নিশ্বাস লক্ষ যোজন দূরে নিঃসীম শূন্যে মিলিয়ে যায়, মনে হয় না যে ভারতবর্ষ আমাদের বেঁধে রেখেছে। আমাদের বিশাল দেশ, বিরাট আকাশ; আমরা কোটি তারকার সঙ্গ পেয়ে ধন্য, মানবসংসারের প্রাত্যহিক তুচ্ছতাকে আমরা তুচ্ছ বলেই জানি। আর এরা? এদের কী-বা রাত্রি কী-বা দিন—সমস্ত জীবনটাই একটা non-stop dance কিংবা non-stop flight। ছন্দহীন-যতিহীন-বেতালা জীবন, জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি অশ্রান্ত বন্যাবেগ, এক মুহূর্ত বিশ্রাম করতে বসলে প্রতিযোগীরা লাথি মেরে এগিয়ে যায়, বৃদ্ধ বয়সেও অন্নচিন্তায় অস্থির করে রাখে। দিনের পরে কখন রাত আসে, রাতের শেষ কোনো দিন হয় কি না ঠিক নেই। এদেশের সূর্য সাম্রাজ্য পাহারা দিতে বেরিয়ে স্বরাজ্যে হাজিরা দেওয়ার সময় পায় না। মাটি ও আকাশের মাঝখানে মেঘ ও কুয়াশার প্রাচীর। মানুষের প্রাণের কথা তারালোকে পৌঁছায় না, ঘরের কোণের ছোটো ছোটো দুঃখ-সুখকে মহাজগতের বড়ো বড়ো দুঃখ-সুখের সঙ্গে মিলিয়ে ধরবার সুযোগ মেলে না, ‘the world is too much with us!’
তারপরে এদের আকাশের আঁধার এদের মনকেও আঁধার করেছে, হাতড়াতে হাতড়াতে যখন যেটুকু সত্য পায় তখন সেইটুকু এদের কাছে সব। এরা কত বড়ো একটা সাম্রাজ্য চালায় নিজেরাই জানে না, সাম্রাজ্য এরা গড়েছে অন্যমনস্কভাবে। খাঁটি প্রাদেশিকতা যাকে বলে তা দ্বীপবাসীতেই সম্ভব এবং আকাশহীন দ্বীপবাসীতে। এরা তিন dimension-এর দ্বীপবাসী। ইংল্যাণ্ডে দলাদলির অন্ত নেই, কিন্তু প্রত্যেক দলই স্বভাবে ইংরেজ অর্থাৎ আকাশহীন দ্বীপবাসী। কোনো একটা আন্তর্জাতিক আন্দোলন ইংল্যাণ্ডে টিকবে না—খ্রিস্টধর্ম টিকল না, সোশ্যালিজম টিকছে না। একদিন যেমন চার্চ অব ইংল্যাণ্ড নিজস্ব খ্রিস্টধর্ম সৃষ্টি করল আজ তেমনি লেবার-পার্টি নিজস্ব সোশ্যালিজম সৃষ্টি করছে। নির্জলা ন্যাশনালিজম ইংল্যাণ্ডেই প্রথম সম্ভব হয়, ইংল্যাণ্ডেই শেষপর্যন্ত স্থায়ী হবে। এর কারণ নৈসর্গিক। তবে নিসর্গের উপরে খোদকারি করছে মানুষ। জাহাজের যা সাধ্যাতীত ছিল এরোপ্লেন তাকে সাধ্যায়ত্ত করছে, channel tunnel হয়তো অসাধ্যসাধন করবে, ইংল্যাণ্ড আর দ্বীপ থাকবে না। কিন্তু মেঘের প্রাচীর?
দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডের নানা স্থানে ঘুরে-ফিরে দেখা গেল। নিসর্গ ও মানুষ মিলে অঞ্চলটাকে সর্বতোভাবে একাকার করে দিয়েছে। একইরকম অগুনতি ছোটো শহর, প্রত্যেকটাতে একই হোটেলের শাখা-হোটেল ও একই দোকানের শাখা-দোকান। স্থানীয় সংবাদপত্র ও থিয়েটারও বহুদূর থেকে চালিত। রেল ও বাস যদিও অগুনতি তবু একই কোম্পানির। একই আবহাওয়া, একইরকম ছিচকাঁদুনে আকাশ, অসমতল ভূমি। মানুষও বাইরে থেকে একইরকম—পোশাকে-চলনে-বুলিতে-আদবকায়দায়; সামান্য যা ইতরবিশেষ তা বিদেশির চোখে স্পষ্ট নয়। ঘন ঘন স্থান পরিবর্তনের ফলে প্রত্যেকটি মানুষ ইংরেজ হয়ে গেছে, প্লিমাথওয়ালা বা টরকিওয়ালা বলে কেউ নেই। অধিকাংশ বাড়িই এখন বাসা, পূর্বপুরুষের ভিটা মাটির মর্যাদা যদি থাকে তো পূর্বপুরুষের গোরস্থান। বাড়ির মালিকরা হয় বাড়িতে থাকেন না, নয় বাড়িতে বোর্ডিং হাউস খোলেন। এইসব শহরের সর্বপ্রধান ব্যবসায় অতিথিচর্যা। অতিথিরা হয় ছুটিতে বেড়াতে আসে, নয় বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজে আসে। যারা স্থায়ীভাবে বসবাস করে তাদেরও দু-ভাগে বিভক্ত করা যায়, তারা হয় দূরস্থিত পিতা-মাতার বোর্ডিং স্কুলে পড়তে-থাকা সন্তান নয় প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের পেনশনপ্রাপ্ত পিতা-মাতা। ছোটোদের জন্যে বোর্ডিং স্কুল ও বুড়োদের জন্যে নার্সিং হোম সমুদ্রতীরবর্তী বহু শত শহরে ও গ্রামে বহুলপরিমাণে বিদ্যমান।
ইংল্যাণ্ড যে দিন দিন socialised হয়ে উঠেছে, এর প্রমাণ ইংল্যাণ্ডের এইসব বোর্ডিং স্কুল, নার্সিং হোম, হাসপাতাল, পাবলিক লাইব্রেরি ইত্যাদি। এসব অনুষ্ঠান জনসাধারণের চাঁদায় চলছে, এসব অনুষ্ঠানে যারা থাকে তারা অনেকসময় জনসাধারণের চাঁদায় থাকে, এসব অনুষ্ঠানের শিক্ষায় বা চিকিৎসায় কোনো একজনের প্রতি পক্ষপাত নেই। গভর্নমেন্টের খরচে চললেও এগুলি এমনিভাবেই চলত। যে-দেশে জনসাধারণ যা গভর্নমেন্টও তাই সেদেশে জনসাধারণের চাঁদায় চালিত বেসরকারি হাসপাতাল ও জনসাধারণের খাজনায় চালিত সরকারি হাসপাতালে তফাত কতটুকু? ইংল্যাণ্ডের অসচ্ছলরা চার্চ প্রভৃতির মধ্যস্থতায় সচ্ছলদের কাছ থেকে যে চাঁদা পায় গভর্নমেন্টের মধ্যস্থতায় সচ্ছলদের কাছ থেকে সেই চাঁদাই পেতে চায়, যদিও তার নাম চাঁদা হবে না, হবে পাওনা। কিন্তু সেই পাওনা ও এই পাওনা তলে তলে একই জিনিস—এমনই বোর্ডিং স্কুলের অপক্ষপাত শিক্ষা, হাসপাতালের অপক্ষপাত চিকিৎসা, নার্সিং হোমের অপক্ষপাত সেবা। এতে আত্মীয়স্বজনের হাত নেই, হৃদয় নেই; এর উপরে সমাজের ফরমাশ প্রবল, ব্যক্তির রুচি-অরুচি ক্ষীণ। সমাজের অলিখিত হুকুমে মা তার কোলের ছেলেকে বোর্ডিং স্কুলে দেয়, রুগণ ছেলেকে হাসপাতালে রাখে। নিজের হৃদয়ের দাবিকে সমাজের দশজনের মতো নিজেও সেন্টিমেন্টাল বলে উড়িয়ে দেয়।
এইসব হোটেল, বোর্ডিং হাউস, স্কুল ও নার্সিং হোম সাধারণত মেয়েদের হাতে। দুধের সাধ ঘোলে মেটাবার মতো এরা home-এর সাধ হোটেলে ও আত্মীয়স্বজনের সাধ অতিথি দিয়ে মেটায়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে একই আদর্শই উদযাপিত হতে চলল। নাম নিয়ে মারামারি করে ফল নেই, এও একরকম সোশ্যালিজম। তলিয়ে দেখলে সোশ্যালিজমের আদত কথাটা কি এই নয় যে, সমাজ ও ব্যক্তির মাঝখানে মধ্যস্থ থাকবে না, সম্পর্কে ও সম্পত্তিতে ‘private’ অঙ্কিত বেড়া থাকবে না? যে-জননী জন্মের পরমুহূর্তে সন্তানকে Dr. Barnardo’s Home-এ ত্যাগ করে ও যে-জননী জন্মের অল্পকাল পরে সন্তানকে বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে দেয় তাদের একজনের সন্তানের খরচা বহন করে বদান্য জনসাধারণ, অপর জনের সন্তানের খরচা বহন করে দূরস্থিত পিতা-মাতা; শিক্ষা উভয়েই পায় আত্মীয়দের অপক্ষপাত তত্ত্বাবধানে, পক্ষপাতী পিতা-মাতার সান্নিধ্য কেউই পায় না অধিকাংশ স্থলে। এদের আর্থিক অবস্থার উনিশ-বিশ থাকলেও এরা সোজাসুজি সমাজের হাতে-গড়া।
প্রবীণাদের মুখে-চোখে কথাবার্তায় এমন একটি স্নিগ্ধতা ও শান্তি লক্ষ করা গেল যা কোনো দেশ-বিশেষের বিশেষত্ব নয়, যুগ-বিশেষের বিশেষত্ব। অস্তগামী চন্দ্রের স্নিগ্ধতার মতো ঊনবিংশ শতাব্দীর স্ত্রী-মুখের স্নিগ্ধতারও দিন শেষ হয়ে এল। এরপরে বিংশ শতাব্দীর স্বতন্ত্রা নারীর প্রখর জ্বালা, লাবণ্যহীন পিপাসাময় দুঃসাহসিক অরুণরাগ। ভারতের কল্যাণী নারীকে ভিক্টোরীয় ইংরেজ নারীতে কত স্থলে প্রত্যক্ষ করেছি, বহু-সহোদরবিশিষ্ট প্রশস্ত গৃহাঙ্গনে এঁদের বাল্যকাল কেটেছে, যন্ত্রমুখর জীবনসংগ্রামে জীবিকার জন্যে এঁরা প্রাণপণ করেননি, পাঁচজনকে খাইয়ে খুশি করেই এঁদের তৃপ্তি, জগতের সামান্যই এঁরা জানেন ও একটি কোণেই এঁদের স্থিতি, উদ্যানলতার ভঙ্গি এঁদের স্বভাবে ও উদ্যানপুষ্পের সুরভি এঁদের আচরণে। অনূঢ়া হলেও এঁরা গৃহিণী নারী, এঁরা স্বতন্ত্রা নারী নন। আর এঁদের পরবর্তিনীরা ফ্ল্যাটে বা বোর্ডিং হাউসে থাকা সাবধানি পিতা-মাতার স্বল্প সহোদরবিশিষ্ট সন্তান। প্রিয়জনের সঙ্গে প্রাত্যহিক দান-প্রতিদান, কলহ-মিলনে যে-শিক্ষা হয়, সে-শিক্ষা অল্পবয়স থেকে বোর্ডিং স্কুলে বাস করে হয়নি। তারপরে জীবিকার দায়িত্ব মাথায় নিয়ে আধুনিক সভ্যতার বেড়াজালে এঁরা যখন হরিণীর মতো ছটফট করেন তখন স্বভাবে আসে বন্যতা, আচরণে আসে ব্যস্ততা এবং বিবাহের সৌভাগ্য ঘটলেও নীরব নিভৃত জীবনে মন বসে না, মন চায় অভ্যস্ত মত্ততা, আগের মতো খাটুনি, আগের মতো নাচ, আগের মতো সন্তানঘটিত দুশ্চিন্তার প্রতি বিতৃষ্ণা, স্বামীঘটিত তন্ময়তার প্রতি অনিচ্ছা। এ নারী গৃহিণী নারী নয়, স্বতন্ত্রা নারী। সমাজের কাজে এর অতুল উৎসাহ, প্রভূত যোগ্যতা—নার্স হিসেবে, শিক্ষয়িত্রী হিসেবে, হোটেলের ম্যানেজারেস হিসেবে, আপিসের সুপারিনটেণ্ডেন্ট হিসেবে এ নারী নিখুঁত। সচিব, সখি ও শিষ্যরূপে এ নারী পুরুষের শ্রদ্ধা জিনে নিয়েছে, আধুনিক সভ্যতার সর্বঘটে বিদ্যমান দেখি যাকে সে-নারী এই স্বতন্ত্রা নারী—গৃহহীন, পক্ষপাতহীন, জনহিতপরায়ণ, সামাজিক কর্তব্যে অটল। এ নারী সব পুরুষের সহকর্মিণী, কোনো একজনের রানি ও দাসী নয়, সকলের সম্মানের পাত্রী, কোনো একজনের প্রেম ও ঘৃণার পাত্রী নয়। কথাটা অবিশ্বাস্য শোনালেও বলতে হবে যে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ধারায় socialisation of women চলেছে, ভারতবর্ষও বাদ যায়নি। এর ফলে কাব্যলোক থেকে প্রেয়সী নারী অন্তর্হিত হল, তার স্থান নিল সঙ্গিনী নারী, passion-এর স্থানে এল understanding।
যুগলক্ষণ থেকে বিচ্ছিন্ন করলে ইংরেজ নারীর কতক বিশেষত্ব আছে—প্রবীণা ও নবীনা এক্ষেত্রে সমান। প্রথমত, ইংরেজ নারী চিরদিনই স্বাধীনমনস্ক, শক্তমনস্ক। ইংরেজ পুরুষও তাই। গুরুজনের ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা মিলিয়ে দেওয়া তার দ্বারা কোনো যুগে হয়নি। সে নিজের ইচ্ছাকে নিজের হাতে রেখে স্বেচ্ছায় সমাজের বাঁধন স্বীকার করেছে, সামাজিক ডিসিপ্লিন মেনেছে। এইজন্যেই বিবাহটা দুজন স্বাধীন মানুষের contract; এতে গুরুজনের হাত পরোক্ষ। দ্বিতীয়ত, নারীত্বের কোনো ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক আদর্শএদেশের নারীর সামনে তেমন করে ধরা হয়নি যেমন আমাদের সীতা-সাবিত্রীর আদর্শ। এর ফলে এদেশের নারী প্রত্যেকেই এক-একটি আদর্শ, কোনো দুজন ইংরেজ নারী কেবল ব্যক্তিহিসেবে নয়, type হিসেবেও এক নয়। সীতা-সাবিত্রীর ছাঁচে ঢালতে গিয়ে আমাদের নারীজাতিকে আমরা সীতা-সাবিত্রী জাতি বানিয়েছি, তাদের মধ্যে নারীত্বের অল্পই অবশিষ্ট আছে। তাই তাদের নিয়ে আরেকখানা রামায়ণ কিংবা মহাভারত লেখা হল না। অথচ হেলেন ও পেনেলোপির পরবর্তিনীদের নিয়ে আজ পর্যন্ত কত কাব্যই লেখা হয়ে গেল, কত ছবিই আঁকা হয়ে গেল। তৃতীয়ত, ইংরেজ নারীর বেশভূষার প্রতি তেমন মনোযোগ নেই যেমন মনোযোগ গৃহসজ্জার প্রতি, শিশুচর্যা বা পশুচর্যার প্রতি। অধিকাংশ ইংরেজ নারীর সাজসজ্জা রূপকথার Cinderella-র মতো। কতকটা এই কারণে, কতকটা অন্য কোনো কারণে অধিকাংশ ইংরেজ নারীরই বাইরের charm নেই। পুরুষের প্রেমের চেয়ে পুরুষের শ্রদ্ধাই এদের কাম্য, সহযোগিতার চেয়ে প্রতিযোগিতার কামনা তীব্র।
১৬
আবহতত্ত্ববিদদের মুখে ছাই দিয়ে আজ আবার সোনার সূর্য উঠেছে, দশ দিক সোনা হয়ে গেছে।
কিছুদিন থেকে এমনই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য প্রতিদিন আমাদের চমক লাগিয়ে দিচ্ছে, এ যেন একটা প্রাত্যহিক miracle। আকাশ উজ্জ্বল নীল, পৃথিবী উজ্জ্বল শ্যাম, গাছেরা এখনও পাতা ফিরে পায়নি কিন্তু ফুলের ভারে ভেঙে পড়ছে, মেঠো ফুলের রঙের বাহার দেখে মনে হয় যেন ফুলের আয়নায় সূর্যের আলোর সব ক-টি রং বিশ্লেষিত হয়েছে। পাখিরাও বসন্তের সঙ্গে দক্ষিণ দেশ থেকে ফিরল, তাদের নহবত আর থামেইনা।
এমনই miracle-এর উপর আস্থা রেখে আমরা মাঝে মাঝে লণ্ডন ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি, যেদিকে চোখ যায় সেইদিকে চরণ যায়, আহার-নিদ্রার ভাবনাটা একাদশ ঘটিকার আগে হাজির হয় না, এবং ভাবনা যদি-বা হাজির হয় আহার-নিদ্রাকে হাজির করানো সেও এক প্রাত্যহিক miracle। মোটের ওপর একটা-কিছু হয়ে ওঠেই ওঠে।
অথচ ওইটুকু অস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে তাল কাটতেও পারিনে। এত বড়ো উৎসব সভায় পান পায়নি বলে খুঁতখুঁত করবে কোন বেরসিক? একসঙ্গে এতগুলো আনন্দ মিলে আক্রমণ করেছে, রং-রূপ-গান-সৌন্দর্যের বাণ সর্বাঙ্গ বিঁধে শরশয্যা রচনা করল। মুখ ফুটে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা নেই, এত অসহায়। স্তবের মতো দেহ-মন লুটিয়ে পড়ে। পরস্পরকে অকারণে ভালোবাসি, অপরিচিতকে হারানো বন্ধুর মতো বুকে টানি। কুয়াশার মতো সংশয়ও উধাও হয়ে গেছে, ফেরার! আকাশব্যাপী আলোর মতো হৃদয়ব্যাপী প্রত্যয় দিবসে সূর্যের মতো, নিশীথে চন্দ্রের মতো জাগরূক। জগতের পূর্ণতা জীবনের অপূর্ণতাকে সমুদ্রের কোলে স্পঞ্জের মতো ওতপ্রোত করেছে। ধন্য আমরা। সৌন্দর্যসায়রের কোটি তরঙ্গাঘাত সইতে সইতে আমরা আছি, আমাদের দুঃখগুলি আনন্দসায়রের বীচিবিভঙ্গ। অভাব? এমন দিনে অভাবের নাম কে মুখে আনবে? আমাদের একমাত্র অভাব বাণীর অভাব—তৃপ্তি জানাবার বাণীর। আদিম মানবেরই মতো অন্তিম মানবও বাণীর কাঙাল থেকে যাবে, কৃতজ্ঞতা জানাবার বাণীর। সেইজন্যেই তো মানুষের মধ্যে কবি সকলের বড়ো—ঋষির চেয়েও, বীরের চেয়েও, ব্যবস্থাপকের চেয়েও, ক্ষুধা নিবারকের চেয়েও, লজ্জা নিবারকের চেয়েও। কবিকে বাদ দিলে সুন্দরের সভায় মানুষ বোবা, কবিকে কাছে রাখলে তার কথা ধার নিয়ে মানুষের মান থাকে। নইলে ঋষি থেকে ক্ষুধা নিবারক পর্যন্ত কেউ একটা পাখির সম্মানও পেতেন না।
শরৎকালে সেকালের রাজারা দিগবিজয়ে যেতেন, বসন্তকালে একালের আমরাও দিগবিজয়ে যাই। আমরা যাই কোনদিকে কোন আপনার লোক অচেনার মতোআত্মগোপন করে রয়েছে তাদের মুখোশ খসাতে। এমন দিনে কি কেউ কারুর পরহতে পারে? এ কি কুয়াশা-কালো দিন যে শত হস্ত দূরের মানুষকে শৃঙ্গী বলে ভ্রম হবে? নিজের দুধের বাটিতে মুখ ঢেকে ভাবব পৃথিবীসুদ্ধ লোক আমাকে দেখে হিংসায় জ্বলেপুড়ে মরছে? না, বসন্তকালে আমাদেরও মুকুল খোলে, আমরা ভালোবাসার সীমা খুঁজতে ফুলের গন্ধের মতো দিশাহারা হই, কোনো শহর থেকে কোনো গ্রামে পৌঁছাই, কোনো তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে কোনো বেড়া টপকাই, কোনো গাছের তলায় শুয়ে কোনো কোকিলের গলা শুনি, কোনো চেরির গুচ্ছ চুরি করে কোনো প্রিয়জনকে সাজাই, অতি অপরিচিত শিশুর গায়ে চকোলেটের ঢিল ছুড়ে ভাব করি। এটা আমাদের দোষ নয়, ঋতুর দোষ। নইলে আমাদের মতো কাজের লোকেরা কি টাইপরাইটারের খটখটানি ফেলে মোরগের কুক-রু-কু-উ শুনতে যায়, না রাজারা রংমহল ছেড়ে রণক্ষেত্রে রং মাখতে যায়?
শীতকালের ইংল্যাণ্ড যদি নরকের মতো, গ্রীষ্মকালের ইংল্যাণ্ড স্বর্গের মতো। প্রতিদিন হয়তো সূর্য ওঠে না, উঠলেও প্রতি ঘণ্টায় থাকে না, কিন্তু তাতে কী? ফুলের মধ্যে তার রং, পাতার মধ্যে তার আলো, পাখির গলায় তার ভাব জমা থাকে; মেঘলা দিনে ওই সঞ্চয় ভেঙে খরচ করতে হয়। ইংল্যাণ্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রথম কথা তার গড়ন। ইংল্যাণ্ড বন্ধুরগাত্রী। যেকোনো একটা ছোটো গ্রামে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকালে কী দেখি? দেখি যেন একখানা concave আয়না। রেখার উপরে রেখা হুড়মুড় করে পড়েছে। অসমতল বললে ঠিক পরিচয়টি দেওয়া হয় না। বলতে পারি অযুত সমতল। সমতলের সঙ্গে সমতল মিলে অযুত কোণ রচনা করেছে, এবং এক কাঠা জমিকেও সমতল রাখেনি। যেটুকু সমতল দেখা যায় সেটুকু মানুষের কুকীর্তি। সুখের বিষয় ইংল্যাণ্ডের সমাজের মতো ইংল্যাণ্ডের মাটিকেও মানুষ সরলরেখা দিয়ে সরল করেনি। এই এক কারণে শীতকালেও ইংল্যাণ্ড অসুন্দর বা অস্বাস্থ্যকর হয় না, হয় কেবল অন্ধকার। শীত-গ্রীষ্ম সব ঋতুতেই ইংল্যাণ্ডে বর্ষা। কিন্তু বর্ষার জল দাঁড়াবার মতো একটু সমতল খুঁজে পায় না।
দেশের মাটির সঙ্গে মানুষের মনের যোগাযোগ বোধ হয় কথার কথা নয়। প্রাণী সৃষ্টির একটা স্তরে মানুষ ও উদ্ভিদ একই পর্যায়ভুক্ত নয় কি? আমার মনে হয় ইংরেজের মন যে law and order-এর জন্যে এত ব্যাকুল, এর কারণ তলে তলে সে তার মাটির মতো law and order-হীন, অযুত সমতল। ইংল্যাণ্ডের মাটির উপরকার জল যেমন অহরহ সমতল পাওয়ার চেষ্টা করছে—পাচ্ছে না; ইংরেজের সমাজও তেমনি যুগে যুগে সাম্যের চেষ্টা করে এসেছে—পায়নি। Snobbery ইংরেজ সমাজের মজ্জাগত, উপরতল না হলে তার সামাজিক রথ গড়িয়ে গড়িয়ে চলতে পারে না। অথচ সাম্যকেও তার মন চায়; নইলে চেষ্টা থাকে না, সবই আপনা-আপনি ঘটতে থাকে, উপরের জল চোখ বুজে নীচে যায়, নীচের ধোঁয়া চোখ বুজে উপরে ওঠে। এমনই নিশ্চেষ্টতা আমাদের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে আমাদের সামাজিক রথ কোনোমতে চলছে ও কোনোমতে থামবারও নয়। হিন্দুর মরণ নেই, সে হিন্দু বিধবার মতো টিকে থাকবেই।
ইংরেজের মনের ভিত্তি অস্থির, সে যেন পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছেছে। সেখানে সবই বিশৃঙ্খল, সবই আগুন! অবচেতনভাবে সে ঝড়ঝঞ্ঝাকে ভালোই বাসে, সমস্যার অভাব সইতে পারে না। কিছু না হোক একটা crossword puzzle তার চাই-ই, কোনোরকম একটা যুদ্ধ—হোক-না-কেন ‘যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ’—না থাকলে সে বেকার। ‘হরি হে, কবে শান্তি ও শৃঙ্খলা পাব’, এটা তার চেতনার কথা। তার অবচেতনার কথা কিন্তু ‘শান্তি ও শৃঙ্খলাকে পাওয়ার চেষ্টা যেন কোনো দিন ক্ষান্ত না হয়, এমনি চলতে থাকে।’ ইংল্যাণ্ডের একটা হাত সমস্যার সৃষ্টি করে, আরেকটা হাত সমস্যার ধ্বংস করে, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে উভয়ের মধ্যে ষড়যন্ত্র না থাকলেও অন্তরালে দুই হাতের একই স্বার্থ—তারা পরস্পরের অন্তর টিপুনি অনুসারে সমস্যার বাড়তি-কমতি ঘটায়, মীমাংসা কাঁচা-পাকা রাখে। আফিসের দুই চালাক কর্মচারী তারা, অদরকারি বলে কোনো দিন তারা বেকারের দলে পড়ল না। ইংল্যাণ্ডকে দেখলেই মনে হয়, শাবাশ, খুব খাটছে বটে, কী ব্যস্ত! কিন্তু তদারক করলে ধরা পড়ে যায়, সমস্যা ও মীমাংসার উপরে যে একটা স্তর আছে সে-স্তরে কি এদেশ কোনো দিন উঠবে! সাত্ত্বিকতার শিবনেত্র কি কখনো এর ললাটে জ্বলবে! এ যে সব পর্যবেক্ষণ করে, কিছুই দেখে না; সব জ্ঞাত হয়, কিছুই জানে না; সব বোঝে, কিছুই উপলব্ধি করে না। এর জীবন যেন জীবনব্যাপী ছেলেমানুষি। সাড়ে তিন থেকে সাড়ে তিন কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত লাট্টুর সঙ্গে লাট্টুর মতোই ঘুরছে!
প্রকৃতি যখন উৎসবময়ী সাজে, মানুষ তখন তার সাজ দেখবার জন্যে কাজকর্ম ফেলে রাখে; এইজন্যে আমাদের বারো মাসে তেরো পার্বণ। ইংল্যাণ্ডেও নাকি এককালে মাসে মাসে দোল-দুর্গোৎসব ছিল, কিন্তু তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ। এখন প্রতিরাত্রে পার্বণ চলে নাচঘরে ও সিনেমায়, প্রতিদিন খেলার মাঠে। বড়োদিন বা ইস্টার এখন নামরক্ষায় পর্যবসিত। ভারতবর্ষের লোকের কাছে এই হিসেবে ইংল্যাণ্ড অত্যন্ত নিরানন্দ দেশ। এদেশে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ পূজ্যের সঙ্গে পূজারির সম্বন্ধ থেকে কখন নেমে এসে শিকারের সঙ্গে শিকারির সম্বন্ধে দাঁড়িয়েছে। এখনকার আমোদপ্রমোদগুলো যেন যুদ্ধে জিতে শত্রুর মৃতদেহের উপরে মাতলামি করা। এখন আমাদের শিরায় শিরায় ভয়, মৃত্যুভয়-দারিদ্র্যভয়-ব্যাধিভয়। প্রকৃতির প্রতিশোধগুলোর নামে মানুষ বিবর্ণ হয়ে যায়। প্রকৃতি যে কতরকমে প্রতিশোধ নিতে আরম্ভ করেছে হিসাব হয় না। একটা মস্ত প্রতিশোধ হচ্ছে যুদ্ধ। আধুনিক কালে আমরা অধিকাংশই রুটিন দেখে স্কুলে পড়ি, অফিসে কাজ করি, খেলতে যাই ও তামাশা দেখি। প্রত্যেক দেশেই এখন হাজার হাজার স্কুল-কলেজ, লাখে লাখে অফিস, কারখানা, সংখ্যাতীত সিনেমা, নাচঘর। প্রত্যেকটি মানুষ হয় সরকারি নয় বেসরকারি ব্যুরোক্রাট—সরকারি ডাকঘরের মেয়ে কেরানি থেকে Lyons-এর চায়ের দোকানগুলোর কর্মচারিণী পর্যন্ত কেউ বাদ যায়নি। এই কোটি কোটি মৌমাছির চিত্তবিনোদনের জন্যে একই অভিনেতা-অভিনেত্রী একাদিক্রমে তিনশো রাত একখানি নাটক অভিনয় করে যান। তিনশো বার বাজালে একখানা গ্রামোফোনের রেকর্ডেরও ইজ্জত থাকে না, কিন্তু ধন্য এদের গলা!
এর পরিণাম জীবনে বিরক্তি। ছুটির দিন সস্তা টিকিট কিনে ট্রেন বোঝাই করে একই স্থানের পাশাপাশি হোটেলে যখন হাজার হাজার জন অভ্যাগত টমাস কুকের তর্জনী সংকেতে পরিচালিত হন ও charabanc-এর পিঠে চড়ে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করতে যান তখন অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি দুজনেই ত্রাহি ত্রাহি করে ওঠেন। তাঁরা বলেন, ‘রুটিনের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করো, মানচিত্রের হাত থেকে, এস্টিমেটের হাত থেকে।’ তখন এমন কোথাও যাওয়ার জন্যে মানুষ ছটফট করে যেখানে টমাস কুক নেই, পাকা সড়ক নেই, শোবার ঘরওয়ালা মোটর কোচ নেই—এককথায় আমাদের শিশুবর্জিত পশুঅলংকৃত সর্বস্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত ফ্ল্যাটের আরাম নেই। সমস্ত পৃথিবীটা যেমন শনৈঃ শনৈঃ একইরকম হয়ে উঠছে, দেখে মনে হয় টমাস কুক গ্রামে গ্রামে দোকান খুলবে, কাউকে প্রাণ হাতে করে বেহিসেবিভাবে অজানা পথে বিবাগি হতে দেবে না। তখন মানুষের একমাত্র আশা-ভরসার স্থল হবে যুদ্ধক্ষেত্র। সত্যিকারের ছুটি পাওয়া যাবে ঠিক সেইখানেই, সেখানকার কিছুই আগে থেকে জেনে রাখা যাবে না, প্রতি পদেই অকস্মাতের সঙ্গে দেখা।
গত মহাযুদ্ধে যে-ক্ষতি হয়েছে তারই পূরণের জন্যে প্রকৃতি অপেক্ষা করছে; তাই এখনও আমরা যুদ্ধের নামে জিভ কাটছি, মেয়েরা আগামী পার্লামেন্টটাকে Parliament of Peacemakers করবার জন্যে চেষ্টা করছে। কিন্তু যে-শিশুরা গোড়া থেকেই মোহমুক্ত হয়ে বাড়ছে, যাদের কল্পনাকে খোরাক দেবার জন্যে দ্যুলোকে ও ভূলোকেএকটিও অপরিচিত প্রাণী, একটাও অপরিচিত স্থান নেই, সেইসব বাস্তববাদী যখন বড়ো হয়ে দলে দলে সরকারি-বেসরকারি ব্যুরোক্রেসির অন্তর্ভুক্ত হয়ে রুটিন সামনে রেখেকাজ করবে তখন তাদের প্রত্যেকের চোখের সম্মুখে না-হয় ঝুলিয়ে রাখা গেল ‘There is no fun like work’ এবং সোশ্যালিস্টদের দয়ায় তাদের কর্মকাল নাহয় করে দেওয়া গেল দিনে পাঁচ ঘণ্টা, তবু তারা সেই সোনার খাঁচা থেকে উড়ে গিয়ে মরতে চাইবে না কি? অত্যন্ত বেশি সংঘবদ্ধ হওয়ার পরিণাম চিরকাল যা হয়েছে তাই হবে, প্রকৃতি কোনো সংঘকেই টিকতে দেয়নি—না বৌদ্ধ সংঘকে, না খ্রিস্টান সংঘকে। এবং অন্নবস্ত্রের জন্যে যে নতুন সংঘটা প্রতি দেশেই নানা নাম নিয়ে শশীকলার মতো বাড়ছে—সোশ্যালিজম তার শেষ অধ্যায় বটে, কিন্তু তার পরেও উপসংহার আছে এবং সে-উপসংহার তেমন মুখোরোচক নয়।
প্রকৃতির প্রতি ইংরেজের দরদ এখনও লোপ পায়নি, ওয়ার্ডসওয়ার্থের নাতি-নাতনিকে এখনও দেখতে পাওয়া যায়। রাস্তার দু-ধারে গাছ রুইবার জন্যে সমিতি হয়েছে, উদ্যান-নগর বা উদ্যান-নগরোপান্ত (Garden Suburb) রচিত হচ্ছে, পল্লির সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রাখবার আন্দোলন তো কবে থেকে চলে আসছে, কিন্তু রেলগাড়িওয়ালা, মোটরগাড়িওয়ালা ও নতুন বাড়িওয়ালাদের লুব্ধদৃষ্টির উপরে ঘোমটা টেনে-দেওয়া পল্লিসুন্দরীর ক্ষমতার বাইরে।* দু-পাঁচজন অসমসাহসিক স্বপ্নদ্রষ্টা পল্লির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে দেশের নব সভ্যতাকে আবাহন করতে ব্যগ্র, কিন্তু হাটের কোলাহলে তাঁদের কন্ঠস্বর বড়োই ক্ষীণ। পলিটিশিয়ানদের কাছে তাঁরা আমল পান না, কেননা পলিটিশিয়ানরা হয় বড়ো বড়ো কলকারখানাওয়ালাদের তাঁবেদার, নয় কলকারখানার শ্রমিকদের সর্দার। দুই দলের স্বার্থই আরও অধিকসংখ্যক কলকারখানা, পাকা সড়ক, নতুন বাড়ি ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত। বেকারসমস্যা দূর করবার জন্যে এরা যা হাতের কাছে পাচ্ছে তা-ই করতে উদগ্রীব, দশ বছর পরে তার ফলে দেশের চেহারাটা কেমন হবে তা ভাবতে গেলে ভোট পাওয়া যায় না, ক্ষুধিতের ক্ষুধাও বাড়তে থাকে। এমনিই তো দেশটাতে জমি যত আছে রাস্তা তার বেশি, রাস্তা যত আছে বাড়ি তার বহুগুণ; আরও দশ বছর পরে দেখা যাবে যে সারা ইংল্যাণ্ডটা একটা বিরাট শহর, এবং এই শহরের লোক নিজেদের খাদ্য নিজেরা একেবারেই উৎপাদন করে না। বলা বাহুল্য সোশ্যালিস্টরা শহুরে শ্রমিকদের ভোটের উপর নির্ভর করে; গ্রাম্য কৃষকদের জন্যে তাদের মাথাব্যথা নেই। কৃষকদের ভোট পাওয়ার জন্যে অন্যান্য দলের এক-একটা কৃষি-পলিসি আছে বটে, কিন্তু পলিটিশিয়ান-জাতীয় প্রাণীদের কাছে দূরদর্শিতা প্রত্যাশা করা বৃথা, তারা তুবড়ির মতো হঠাৎ জ্বলে হঠাৎ নেভে, তাদের জীবদ্দশা বড়োজোর বছর পাঁচেক। সমগ্র দেশের নব সভ্যতার আবাহন করা তাদের কাজও নয়; তাদের সাজেও না। তাদের একদল আরেক দলের জন্যে বসবার জায়গা রেখে যেতেই জানে, সমস্ত জাতিটার চলার ভাবনা তাদের অতি সূক্ষ্ম মস্তিষ্কে প্রবেশপথ পায় না।
এখনকার ইংল্যাণ্ডকে দেখে দুঃখিত হবার কারণ আছে। সে-কারণ এ নয় যে, ইংল্যাণ্ডের নৌবহরকে আমেরিকার নৌবহর ছাড়িয়ে উঠছে, ইংল্যাণ্ডের উপনিবেশরা পর হয়ে যাচ্ছে, ইংল্যাণ্ডের অধীন দেশগুলি স্বাধীন হয়ে উঠছে, ইংল্যাণ্ডের অন্তর্বিবাদে তার ধনবৃদ্ধি বাধা পাচ্ছে। আসলে সাম্রাজ্যের জন্যে ইংল্যাণ্ড কোনোদিন কেয়ার করেনি, যেমন ঐশ্বর্যের জন্যে চিত্তরঞ্জন দাশ কোনোদিন কেয়ার করেননি। ইংল্যাণ্ড এক হাতে অর্জন করেছে অন্য হাতে উড়িয়ে দিয়েছে, একদিন যাদের ক্রীতদাস করেছে অন্যদিন তাদের মুক্ত করে দিয়েছে, যেদিন আমেরিকা হারিয়েছে সেইদিন ভারতবর্ষ পেয়েছে। পুরুষস্য ভাগ্যম। আধিভৌতিক লাভ-ক্ষতির কথা ইংল্যাণ্ড এতদিন ভাবেনি, এইবার ভাবতে শুরু করেছে; দেখে মনে হয় এবার আর তার সেই পুরাতন অন্যমনস্কতা নেই, এবার সে অক্ষমের মতো নিজের অক্ষমতার কথাই ভাবছে। ব্যাপার এই যে ইতিমধ্যে কবে একদিন—ঊনবিংশ শতাব্দীতেই বোধ হয়—ইংল্যাণ্ডের আত্মা অন্তর্হিত হয়েছে কিংবা জীবন্মৃত হয়েছে। শেক্সপিয়ার থেকে ব্রাউনিং পর্যন্ত এসে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। যে-ইংরেজের প্রাণ ছিল adventure বা বিপদবরণ, সে এখন মন্ত্র নিয়েছে ‘Safety first’। যা-কিছু এককালে অর্জন করেছে তাই এখন সে নিরাপদে ভোগ করতে চায়। কিন্তু সংসারের নিয়ম এই যে, বীর ছাড়া অন্য কেউ বসুন্ধরাকে ভোগ করতে পারবে না, অর্থাৎ অর্জন করা ও ভোগ করা একসঙ্গে চলা চাই। বস্তুত অর্জন করাটাই ভোগ করা। অর্জিত ধনকে রয়ে-বসে ভোগ করা হচ্ছে সংসারের আইনে চুরি করা। এ আলস্যকে সংসার কিছুতেই প্রশ্রয় দেবে না। যার মাইট নেই তার রাইট তামাদি হয়ে গেছে, যার হজম করবার ক্ষমতা নেই সে খেতে পাবে না।
কিছুকাল থেকে আধিভৌতিক ঐশ্বর্যের ওপরে মন দেওয়া ছাড়া ইংল্যাণ্ডের গত্যন্তর থাকেনি, কেননা মন দেবার মতো আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য তার কখন ফসকে গেছে। এখন আধিভৌতিক ঐশ্বর্যও যায়-যায় দেখে তার মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছে। ধনকে যে-মানুষ পরমকাম্য মনে করে কোটিপতি হল, সে যখন দেখে যে আরেক জন কেমন করে দ্বি-কোটিপতি হয়েছে তখন সে চোখে আঁধার দেখে, তার পা টলতে থাকে। ভদ্রলোকের ছেলে যখন ইতর লোকের ছেলের সঙ্গে কথাকাটাকাটি করতে যায় ও একটি অশ্লীল কথা বলতে গিয়ে দশটি শুনে আসে, তখন তার যে-অবস্থা হয় ইংল্যাণ্ডের অনেকটা সেই অবস্থা। ধনবলকে সে সকলের থেকে শ্রেয় মনে করেছিল, আজ ধনবলে সে প্রথম থাকতে পারছে না। আমেরিকা তার চেয়ে বড়ো Power হয়ে ‘জগৎ গ্রাসীতে করেছে আশয়’। ইংল্যাণ্ডের এই অপমান এখনও তার মর্মে বেঁধেনি, কিন্তু চামড়ায় বিঁধছে। বেশ একটু inferiority complex তার মধ্যেও লক্ষ করছি। ভারতবর্ষের মতো সেও বলতে আরম্ভ করেছে, ‘আমি বড়ো গরিব, আমি গোবেচারা’, কিন্তু সংসারের আইনে গরিব হওয়া হচ্ছে ফাঁসির আসামি হওয়া। হয় আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যে ধনী হতে হবে, নয় আধিভৌতিক ঐশ্বর্যে ধনী হতে হবে, অস্তিত্বের মূল্য দেওয়ার জন্যে ধনী না হলে চলে না।
১৭
কেবলমাত্র সূর্যের আলোর দ্বারা একটা দেশের কতটা পরিবর্তন ঘটতে পারে তার সাক্ষী গ্রীষ্ম কালের ইংল্যাণ্ড। মাটি তেমনি আছে, মানুষ তেমনি আছে, সভ্যতার জগন্নাথের রথ তেমনি উদ্ভ্রান্ত গতিতে চলেছে; কিন্তু মেঘ-কুয়াশার কপাট যেই খুলল অমনি দেখা দিল সূর্যলোক-চন্দ্রলোক-নক্ষত্রলোক। ইংল্যাণ্ড ছাড়াও যে দেশ আছে, সমুদ্রের নজরবন্দি হয়ে মেঘ-কুয়াশার কারাগারে সেকথা আমরা জানতুম না; এখন দেখা গেল আকাশজোড়া অমরাবতী। স্বর্গ আমাদের এত কাছে যে হাত বাড়ালে হাতে ঠেকে, কেবল হাত বাড়ানোটাই শক্ত, কেননা হাত দিয়ে যে আমরা মাটি আঁকড়ে থাকতেই ব্যস্ত।
এমনই মধুর গ্রীষ্মকালে কেমন করে মানুষের যুদ্ধে মতি হয় অনেকসময় আশ্চর্য হয়ে ভাবি। শীতের অন্ধকারে শরীরটাকে গরম রাখবার জন্যে পরস্পরের শরীরেবেয়নেটের চিমটিকাটা ও পরস্পরের মুখ দেখবার জন্যে বারুদে আগুন-ধরানো, এর অর্থ বুঝতে পারি। কিন্তু বসন্ত কালে, গ্রীষ্ম কালে, শরৎ কালেও অরসিকের মতো যুদ্ধ করতে কেমন করে ইউরোপের লোকের প্রবৃত্তি হল? আকাশের দিকে নির্নিমেষ চেয়ে দিনের পর দিন যায়, তবু তার রহস্যের কূল পাওয়া যায় না। সে আমাদের নিত্যবিস্ময়।পাখিগুলো যে কেন সারাবেলা গান গেয়ে মরে, এত ফুল যে কোন আনন্দে ফোটে, বন ও মাঠ দখল করেও রাজপথের বক্ষ ভেদ করে ঘাস মাথা তোলে কেন, মোটরের দাপাদাপিকে অগ্রাহ্য করে শামুক তার অবসরমতো ঘণ্টায় দশ ইঞ্চি অগ্রসর হয় কেন, এই অপরূপ শহরটাকে কেন এমন অপূর্ব দেখায়, কলকারখানার কলঙ্ক নিয়েও কেন ইংল্যাণ্ড এখনও অম্লানযৌবনা—এসব ধাঁধার একমাত্র জবাব সূর্যের করুণা।
সূর্য অভয় দিয়ে বলছে, পৃথিবীকে তোমরা যত খুশি কুৎসিত, যত খুশি দুঃখময়, যত খুশি বিশৃঙ্খল করো-না কেন আমি আছি তার সুখ-সৌন্দর্য-শৃঙ্খলার কুবের-ভান্ডারী, আমি তাকে সোনা করে দেব।
সূর্য আমাদের বিনা মূল্যের বিমা কোম্পানি। যখন যা হারায় তা গড়িয়ে দেয়। জীবন হারালেও জীবন ফিরিয়ে দেয়। সূর্যের assurance শুনলে তাই ফুল-পাখি-ঘাস-শামুকের মতো আমাদেরও প্রাণে ভরসা আসে, আমরা জীবনকে একটা কানাকড়ির চেয়ে মূল্যবান মনে করিনে, আমরা ওদেরই মতো নিরুদবেগে দিন কাটাই, অকারণে খুশি হই। ওই যে সাদা প্রজাপতিটি, ওর জীবন একটা দিনের—কোথায় ওর মৃত্যুভয়, কোথায় ওর জীবনের মূল্য, কোথায় ওর অপ্রিয় কর্তব্য? খোলা আকাশের জানলা দিয়ে সভ্য মানুষের অর্থহীন হট্টগোল ও আর্তনাদ সুতো-ছেঁড়া ফানুসের মতো কোথায় উড়ে গেল।
এমন দিনে চোখ-কান-মন খোলা রেখে বেড়াতে বেরিয়ে সুখ আছে। যা-ই দেখি তা-ই নতুন মনে হয়, আশ্চর্য মনে হয়। রাস্তার এক কোণে দুই বুড়ি বসে ফুল বেচছে। অত ফুল তারা পেল কোথায়? সব ফুলের কি তারা নাম জানে, মর্ম বোঝে, যত্ন জানে? শাকসবজির হাট; নানা দেশের ফল-পাতা জাহাজে করে গাড়িতে করে এসেছে। গাড়ি সেই মান্ধাতার আমলের টাট্টুঘোড়ার গাড়ি, গাধার গাড়ি। মোটরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার গাড়োয়ান দুরুচ্চার শব্দ করে চলেছে, তার হাঁটু থেকে পা অবধি একটা পাটের থলে কম্বলের কাজ করছে, তার অলক্ষিতে কখন একটা ছোঁড়া গাড়ির পেছন ধরে ঝুলে পড়েছে। হাটের কাছে অপেরা হাউস, রাত্রে Chaliapine অপেরায় নামবেন, সকাল থেকে লোক জমে গেছে; একখানা ক্যাম্বিসের চেয়ার ভাড়া করে এক-একজন বসে গেছে সন্ধ্যা বেলা কখন টিকিটঘর খুলবে তারই প্রতীক্ষায়; কেউ সংগীতের স্বরলিপি নকল করছে; কেউ বই পড়ছে; কেউ গল্প করছে; কেউ-বা চেয়ারের উপর নিজের নামের কার্ড এঁটে দিয়ে অফিসে গেছে কিংবা বেড়াতে গেছে। কাছেই ড্রুরি লেনের থিয়েটার—কবেকার থিয়েটার—গ্যারিক ও সেরা সিডন্স একশো-দেড়শো বছর আগের মানুষ। ইংল্যাণ্ডের থিয়েটারগুলোর অধিকাংশই অত পুরোনো নয়, কিন্তু প্রত্যেকের পিছনে বহু শতাব্দীর রুচি ও সাধনা রয়েছে—এক অভিনেতার থেকে আরেক অভিনেতায় সংক্রামিত, লুপ্ত থিয়েটার থেকে চলিত থিয়েটারে হস্তান্তরিত। সেইজন্যে ইংল্যাণ্ডের থিয়েটার এক-একটা যুগে খুব উঁচু দরের না হলেও কোনো যুগেই নীচু দরের হতে পারে না, আগের যুগের আদর্শ তাকে পাঁক থেকে টেনে তোলে। ফ্রান্সের থিয়েটার আরও পুরাতন, ফ্রান্স যতদিনের থিয়েটার ততদিনের। সে যেন জাতির ধমনি। তার স্বাস্থ্যনাশ জাতির স্বাস্থ্যনাশের শামিল। ঘোরতর রাষ্ট্রবিপ্লবের দিনে, মহাযুদ্ধের দিনেও ফ্রান্সের থিয়েটারে লোকারণ্য। ইংল্যাণ্ডের থিয়েটার তার অতখানি নয়—ইংল্যাণ্ডের ধমনি তার ক্রিকেট খেলার মাঠ, তার ঘোড়দৌড়ের মাঠ।
কাছেই হাই কোর্ট। হাই কোর্টটি যেকোনো ভারতবর্ষীয় হাই কোর্টের চেয়ে ছোটো ও জনবিরল। ইংরেজের দেশে স্পেকটাকুলার কিছুই নেই, এক যুদ্ধজাহাজ ছাড়া। তাই ভারতবর্ষের লোক লণ্ডনে এসে বিষম খেপে যায়—এই তো দেশ, এই তো মানুষ, এই তো দৃশ্য, এই তো খাদ্য, এই দেখতে এতদূর আসা! লণ্ডনের অর্ধেকের বেশি লোক অকথ্য বস্তির বাসিন্দা, মেফেয়ারের অদূরেই ওয়েস্টমিনস্টারের বস্তি, পার্লামেন্টের প্রদীপ যেখানে জ্বলছে সেইখানেই আঁধার। মেফেয়ারও এমন-কিছু আহামরি নয়, আমাদের মালাবার হিল ওর থেকে ঢের বিলাসযোগ্য। বিলেত দেশটা মাটির বলে মাটির! ব্যাঙ্ক পাড়াতে বেড়াতে যাও—কলকাতার ক্লাইভ স্ট্রিটের দোসর। টেমস নদীর চেহারা তো জানই—সিন্ধুপ্রদেশে বোধ করি ওর থেকে বড়ো বড়ো নালা আছে। লণ্ডনের বাগানগুলো দেখে একজন লাহোরবাসীর নাক-সঁিটকানো দেখবার মতো। উত্তর ভারতের যেকোনো তৃতীয় শ্রেণির মসজিদ ও দক্ষিণ ভারতের যেকোনো তৃতীয় শ্রেণির মন্দির ইংল্যাণ্ডের ক্যাথিড্রালগুলোকে হার মানায়। রাজবাড়ির তুলনা ভারতবর্ষে অন্তত ছশো বার মিলবে, কেননা ভারতবর্ষের সামন্ত রাজারা ক্ষমতায় যা-ই হন, জাঁকজমকে এক-একটি চতুর্দশ লুই। পঞ্চম জর্জ তো তাঁদের তুলনায় একটি অধ্যাপক ব্রাহ্মণ।
ভারতবর্ষের লোক সাইটসিইয়ার হিসেবে ইংল্যাণ্ডে এলে ঠকে যাবে। সিনেমা দেখাই যদি অভিপ্রায় হয় তবে দেশে সিনেমা স্থাপন করতে তো বেশি খরচ লাগে না। বিদ্যালাভের জন্যে যদি আসতে হয় তবে এত দেশ থাকতে কেবল ইংল্যাণ্ডে কেন? হ্যাঁ, ব্যবসা করতে আসা একটা কাজের কথা বটে। কিন্তু তা করতেও গোটা দুনিয়া পড়ে আছে।
তবু ভারতবর্ষের লোকের সব দেশের চেয়ে বেশি করে ইংল্যাণ্ডেই আসা উচিত, এবং সব দেশের লোকের চেয়ে ভারতবর্ষের লোকেরই ইংল্যাণ্ডে আসা বেশি দরকার। ভারতবর্ষ ও ইংল্যাণ্ড চরিত্রের জগতে antipodes। ইংল্যাণ্ডের যে-গুণগুলি আছে ভারতবর্ষের সেই গুণগুলি নেই, এবং ভারতবর্ষের যে-গুণগুলি আছে ইংল্যাণ্ডের সেই গুণগুলি নেই। এই একই কারণে এত দেশ থাকতে ইংল্যাণ্ডে ও ভারতবর্ষে যোগাযোগ ঘটল। এবং এই এক কারণে স্বাধীন ভারতবর্ষকেও সাম্রাজ্যহীন ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ রক্ষা করতে হবে। ফ্রান্স-জার্মানি-রাশিয়া কম-বেশি ভারতবর্ষেরই মতো। তাদের কাছ থেকে ভারতবর্ষের শেখবার আছে অনেক কিন্তু তাদের চরিত্র ভারতবর্ষের চরিত্রের সঙ্গে এত মিলে যায় যে তাদের চরিত্র থেকে ভারতবর্ষের আয়ত্ত করবার আছে অল্পই। অন্য কথায় তারা ভারতবর্ষের সগোত্র, তাদের সঙ্গে বিবাহ বড়ো বেশি ফল দেবে না। ইংল্যাণ্ডের গোত্র আলাদা। ভারতবর্ষ সবাইকে ঘরে টানে, ইংল্যাণ্ড সবাইকে পথে বার করে। ইংল্যাণ্ড খোঁজায়, ভারতবর্ষ খোঁজার শেষ বলে দেয়। ইংল্যাণ্ড প্রশ্ন, ভারতবর্ষ উত্তর। ব্রিটানিয়া নিষ্ঠুরা স্বামিনী—তাকে খুশি করবার জন্যে প্রাণ হাতে করে জাহাজ ভাসাতে হয়, হয় রত্ন নিয়ে ফিরে আসা, নয় প্রাণ হারিয়ে দেওয়া, নয় উপনিবেশ গড়ে ফিরে আসবার নাম না করা। ভারতবর্ষ করুণাময় ঋষি গৃহস্থ—ক্রৌঞ্চ পাখিকে সান্ত্বনা দেয়, স্বামীবর্জিতাকে আশ্রয় দেয়, যে আসে সে-ই তার স্নেহের অতিথি। একের চরিত্রের চিরবিপদবরণস্পৃহা অপরের চরিত্রের সহজ শান্তির সঙ্গে সমন্বিত হবে, এই অভিপ্রায় উভয়ের বিধাতার মনে ছিল। ইতিহাস তো একরাশ আকস্মিকতা নয়। আকাশের এক কোণে বাতাসের অভাব ঘটলে অন্য কোণ থেকে যেমন বাতাস ছুটে যায়, ভারতবর্ষকে পরিপূর্ণতা দিতে ইংল্যাণ্ড তেমনি ছুটে গেছে। অন্য দেশ যায়নি, কারণ অন্য দেশ ভারতবর্ষেরই মতো। অন্য দেশ গিয়ে ফিরে এসেছে, কারণ অন্য দেশকে ভারতবর্ষের দরকার ছিল না।
একথা ঠিক যে ফ্রান্স যদি ভারতবর্ষের হাত ধরত তবে ভারতবর্ষের সঙ্গে তার মনের অমিল ঘটত না, যেমন ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ঘটেছে। কিন্তু তা হলে ভারতবর্ষের চরিত্র কোনোদিন পূর্ণতা পাওয়ার সুযোগ পেত না। ফ্রান্স যে-দেশে গেছে সেদেশকে ফ্রান্সে পরিণত করেছে, সেদেশকে বলেছে—তোমরাও ফরাসি, তোমরাও স্বাধীন। এ বাণীর সম্মোহন কোনো দেশ এড়াতে পারেনি। ফ্রান্সের দখলে থাকলে আমরা কেউ কেউ ফ্রান্সের সেনাপতি হয়ে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট বা সম্রাটও হতে পারতুম, যেমন কর্সিকাবাসী ইটালিয়ানবংশীয় নেপোলিয়ন একদিন হয়েছিলেন। কেবল নিজেকে ফরাসি বলে ঘোষণা করতে হত, এই যা কষ্ট। ফরাসিরা অনেকটা মুসলমানদের মতো ডেমোক্র্যাটিক; তাদের দলে ভরতি হওয়া খুব সোজা এবং ভরতি হলে আর পালাতে ইচ্ছে করে না। ভারতবর্ষের মুসলমান আরব দেশের মুসলমানের কাছ থেকে কীই-বা পেয়েছে শুধু নামটা ছাড়া! তবু সেই নামটাকে পাসপোর্ট করে সে পৃথিবীর সব দেশে সমনামাদের প্রীতি পায়। ফরাসি নামটারও তেমনি মহিমা। এই নাম নিয়ে আমরা এত দিনে ভারতবর্ষের মানচিত্রের উপরে লিখতুম ‘ফ্রেঞ্চ রিপাবলিকের কয়েকটা জেলা’—যেমন আলসাস বা লোরেন তেমনি বাংলা বা অসম।
সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা সবই আমরা পেতুম, ফ্রান্স থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা স্বপ্নেও ভাবতুম না। কিন্তু আমাদের কোনো বৈশিষ্ট্যকেই ফ্রান্স আমল দিত না, ফ্রান্সের লজিকপ্রিয় মগজ অসংগতি সহ্য করতে পারে না। সম্ভবত ফরাসিরা আমাদের দেশে একটিও দেশীয় রাজ্য থাকতে দিত না, ভারতবর্ষের মানচিত্রখানা আঁকবার পক্ষে সোজা হত। হিন্দু-মুসলমান আইনের বদলে চালাত কোড নেপোলিয়ন। এককথায় আমাদের ভারতীয়ত্বটুকু কেড়ে নিয়ে আমাদের দিত তার চেয়ে অনেক সুবিধাজনক ফরাসিত্ব।
কিন্তু গোড়ায় গলদ, ফ্রান্স কোনোদিন ভারতবর্ষ নিতেই পারত না। কেননা ফ্রান্সের চারিত্রিক দোষ-গুণ মোটের উপর আমাদের কাছাকাছি। ফরাসিরা গৃহপ্রিয়, দেশ ছেড়ে বেরুতেই চায় না, বড়োজোর খিড়কির কাছে আফ্রিকা পর্যন্ত ওদের গতিবিধি। ইন্দোচীন প্রভৃতি খুচরো উপনিবেশগুলোকে ধর্তব্য মনে করলে ফিজি প্রভৃতি জায়গায় আমাদের উপনিবেশকেও ধরতে হয়। গৃহপ্রিয় মানুষের স্বভাব ঘরের লোকের সঙ্গে দু-বেলা ঝগড়া করা, চক্রান্ত করা, সন্ধি করা ও পাশাপাশি থাকা। ফ্রান্সের প্রতিনিধিসভায় যতগুলো চেয়ার ততগুলো দল। ফ্রান্সের সাহিত্যরাজ্যেও যতগুলি লেখক ততগুলি পত্রিকা, যতগুলি পত্রিকা ততগুলি দল। কোনো একটা দলের সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকলে লেখককে লোকে অজ্ঞাতকুলশীল ভেবে খাতিরই করতে চায় না। ফ্রান্স পরিবারপ্রধান দেশ। পরিবারের সঙ্গে জড়িত না হলে, পরিবারের ভার মাথায় না নিলে, ব্যক্তিকে সে ব্যক্তিই মনে করে না। ইংল্যাণ্ড ব্যক্তিকে চরে বেড়াবার পক্ষে যথেষ্ট মুক্তি দিয়েছে, John Bull ষাঁড়ই বটে, তার পারিবারিক দায়িত্ব সামান্য। তাই ইংরেজের ব্যক্তিত্ব একলা মানুষের ব্যক্তিত্ব। কিন্তু ষাঁড়েরও গোষ্ঠ থাকে, বৃহৎ গোষ্ঠ। ইংরেজের বৃহৎ ক্লাব বৃহৎ পার্টি। বৃহৎ পার্টির একজন না-হলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব এদেশে নগণ্য এবং তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব অক্রিয়। এদেশের মাটিতে আকাশকুসুম যদি-বা জন্মায় তবে সে নেহাত আগাছা, তাকে উপড়ে ফেলবার আগেই সে মানে মানে সরে পড়ে। Shelley ইটালি প্রয়াণ করলেন। Bertrand Russel আমেরিকা প্রয়াণ।
ইংল্যাণ্ডের চরিত্রের আরেকটা গুণ, তার চরিত্র মুহুর্মুহু বদলায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশের ইংরেজ বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশের ইংরেজকে দেখলে প্রপৌত্র বলে চিনতে পারবে না। এরা আরেক জাতি। তিন পুরুষের ব্যবধানে সমাজে ও রাষ্ট্রে বিপ্লব ঘটে গেছে। কিন্তু চাকার তলার দিকটা কখন উপরের দিক হয় চাকা তা জানে না, চাকা ঘুরতেই ব্যাপৃত। প্রতিদিন একটু একটু করে বিপ্লব চলেছে; চোখে পড়ে না এইজন্যে যে চোখও বিপ্লবের অঙ্গ।Galsworthy-র নতুন নাটক Exiled-এ নীচের ধাপের লোক উপরের ধাপে উঠল, Galsworthy-একে ঠাট্টা করে বললেন, evolutionary process, এবং যারা নবাগতের ধাক্কা খেয়ে উপরের ধাপ থেকে পা পিছলে পড়ল তাদের জন্যে দুঃখ করলেন। কিন্তু তারাও তো evolutionary process-এরই কল্যাণে ভুঁই ফুঁড়ে উপরে উঠেছিল। এখনকার ভুঁইফোঁড়রাও পঞ্চাশ বছর পরে উপরের ধাপ থেকে exiled হবে। তা বলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না, ইংল্যাণ্ড যতই বদলাক ইংল্যাণ্ডই থাকবে, চাকা যতই ঘুরুক চাকাই থাকবে। পুরাতনকে ইংল্যাণ্ড সমীহ করে, কিন্তু নির্বাসিতও করে, অ্যারিস্টোক্র্যাটের প্রতি তার পরম শ্রদ্ধা, কিন্তু পালা করে সবাইকে সে একই গদিতে বসাবে বলে কাউকেই দীর্ঘকাল গদিয়ান হতে দেয় না। পর্বতের চূড়ায় যে-ই ওঠে সে-ই টাল সামলাতে না পেরে আছাড় খায়, অথচ যে-দেশের সমাজের গড়ন পার্বত্য সেদেশে কতকগুলো লোককে চূড়ায় চড়ে চূড়াচ্যুত হতেই হবে। অধিকাংশ অ্যারিস্টোক্র্যাটেরই বংশলোপ হয়, সুতরাং কষ্ট করে তাদের মাথা কাটতে হয় না। স্বাচ্ছন্দ্যের আদর্শ বাড়াতে গিয়ে অতিমাত্রায় জন্মশাসন, তার ফলে বংশলোপ। উচ্চতর মধ্যবিত্তরাও জন্মশাসনপূর্বক নিজেদের সংখ্যা কমাতে লেগেছে, তার ফলে নিম্নতর মধ্যবিত্তরা উচ্চতর মধ্যবিত্ত হয়ে উঠছে। নিম্নতর মধ্যবিত্তদের সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা। নিম্নতর মধ্যবিত্তদের পরিবারে আজকাল তিন-চারটির বেশি সন্তান দেখতে পাওয়া ভার। অতএব শ্রমিক শ্রেণির লোক ক্রমশ নিম্নতর মধ্যবিত্ত হয়ে উঠছে। এই হল evolutionary process, এটা ইংল্যাণ্ডের একটা মস্ত উদ্ভাবন। এতে শ্রেণি বিশেষের লাভ-লোকসান হতে পারে, সমস্ত দেশটার লাভ-লোকসান কিছুমাত্র নেই। পরিবর্তন বিনা কোনো জীবন্ত দেশের জীবন থাকে না, অতএব দু-তিন পুরুষ অন্তর মাথা কাটাকাটি না করে প্রতি পুরুষেই একের নির্বাসন ও অপরের রাজ্যপ্রাপ্তি ভালো না মন্দ? এতে জাতির চরিত্রটাতেও মরচে ধরে না, নতুন গুণাবলি পুরানো গুণাবলিকে মুছে সাফ করে দেয়। পুরোনো অ্যারিস্টোক্রেসির সঙ্গে তুলনা করলে নতুন অ্যারিস্টোক্রেসির কোনো গুণ দেখতে পাও না কি? ভুঁইফোঁড় বলে ঠাট্টা যদি কর, তবে ভুঁইফোঁড়ের ভিতরকার সত্যকে হারাবে। দুটোকে যে একসঙ্গে বহাল করেনি এর কারণ ইংল্যাণ্ড একসঙ্গে দুটো সত্যকে সইতে পারে না। ইংল্যাণ্ডের পাকশাস্ত্রে পাঁচমিশেলি নেই। মাছ-মাংসের সঙ্গে আমরা আলু-কপি মিশিয়ে রাঁধি, একথা শুনে একজন থ হয়ে গেলেন। ‘তাহলে তোমরা মাছের কিংবা মাংসের কিংবা আলুর কিংবা কপির বিশেষ স্বাদটি পাও কী করে?’ এর জবাব—‘তা পাইনে। কিন্তু সমস্তটার সমন্বয়ের স্বাদটি পাই।’
বিপ্লবকে ইংল্যাণ্ড ঠেকিয়ে রাখে প্রতিদিন একটু একটু করে ঘটতে দিয়ে। সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর রেভলিউশন যেমন প্রতিদিনের ব্যাপার অথচ কোনোদিন আমরা খবর পাইনে যে আমরাও সেই রেভলিউশনের ব্যাপারী, ইংল্যাণ্ডেও তেমনি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক রেভলিউশন নিত্যকারের ঘটনা বলে কোনো ইংরেজ টের পায় না কত বড়ো ঘটনায় সে লিপ্ত। টের পেলে সে ঘটতে দেবে না, সেইজন্যে বিপ্লবটাকে কিস্তিবন্দিভাবে ঘটাতে হয়। অ্যারিস্টোক্র্যাটের হাত থেকে শ্রমিকের হাতে শাসনভার আসতে দুশো বছর লেগেছে; স্ত্রীস্বাধীনতার আন্দোলন অন্তত একশো বছরের; দেড়শো বছর ধরে আক্রমণ করেও টাট্টুঘোড়ার গাড়িকে এখনও ঘায়েল করতে পারা যায়নি; চরকা এখনও কোনো কোনো ঘরে ঘরঘর করছে; এবং এমন লোক এখনও অনেক যারা immaculate conception প্রভৃতি খ্রিস্টীয় তত্ত্বে বিশ্বাস হারায়নি। তথাচ ইংল্যাণ্ড কোনোদিন চুপ করে বসে নেই, সে প্রতিদিন ঘর ঝাঁট দিচ্ছে, প্রতিদিন পুরোনো গহনাকে ভেঙে নতুন ফ্যাশনে গড়িয়ে নিচ্ছে। ইংল্যাণ্ডের মন সংস্কারকের মন। পলিটিকসের মতো সব বিষয়েই ইংল্যাণ্ডে একটা চিরস্থায়ী প্রতিপক্ষ (permanent opposition) আছে—ইংরেজ মাত্রেই কোনো-না-কোনো বিষয়ে একজন বিদ্রোহী। আবহমান কাল ইংরেজ মাত্রেই বলে আসছে—‘This state of things must not continue.’ আমাদের বুলির সঙ্গে এ বুলির কত-না তফাত। আরও ভাববার কথা, এ বুলি আবহমান কালের ও প্রতিজনের। ‘Something must be done’—এই হল এ বুলির উপসংহার। একটা নমুনা দিই। সার্কাস ইংল্যাণ্ডে নেই বললেও হয়। তবু সার্কাসে বাঘ-হাতি প্রভৃতি বন্যজীবকে নাচানো অনেকের চোখে নিষ্ঠুর ঠেকে। এখনও ইংল্যাণ্ডের কোনো কোনো জায়গায় খরগোশ শিকার, পাখি শিকার চলে, সেটাও নিষ্ঠুর কাজ। খুনিকে প্রাণদন্ড দেওয়া তো রীতিমতো বর্বরতা। এইসব বন্ধ করবার জন্য পার্লামেন্টকে আবেদন করা চলেছে। এই ধরনের আবেদন প্রতিবছর পার্লামেন্টে পৌঁছায়। Vivisection-এর বিরুদ্ধে লোকমত গড়া বহুকাল থেকে চলে আসছে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, এইসব ছোটোখাটো সংস্কার অত্যন্ত সাধারণ মানুষের অবসর সময়ের উদ্যোগের ফল, মহাত্মা গান্ধীর মতো অসাধারণ লোকের সারা সময়ের কাজ নয়। সমাজ-রাষ্ট্রের এক-একটা চক্রাংশ যদি প্রত্যেকে ঘোরায় তবে সমস্ত চাকাটা বোঁ বোঁ করে ঘোরে, সমাজ-রাষ্ট্র দেখতে দেখতে বদলে যায়, অধ্যবসায়ীর পক্ষে জীবিতকালেই চক্রপরিবর্তন প্রত্যক্ষ করা শক্ত হয় না। প্রত্যেক ইংরেজ মরণকালে এই ভেবে সান্ত্বনা পায় যে, আমিও কিছু-না-কিছু ঘটিয়েছি। অবশ্য খুব বেশি নয়, খুব অসাধারণ নয়, তবু কিছু! আমাদের দেশেও যদি সবাই সামান্য করেও কিছু করত—প্রতিদিন করত—তবে আমাদের অসাধারণ মানুষগুলিকে অহরহ চরকার মতো ঘুরতে হত না, চরকাও ঘোরাতে হত না এবং আমাদের সাধারণ মানুষগুলি করবার মতো কত কাজ পড়ে রয়েছে দেখে ‘কোনটা করি, কোনটা করি’ ভাবতে ভাবতে জীবন ভোর করে দিত না, কিংবা একসঙ্গে সব ক-টাতে হাত দিয়ে সব ক-টা মাটি করত না, কিংবা হাজার বছরের আলস্যের হাজারটা নোঙরকে এক বিপ্লবের ঝড়ে বিপর্যস্ত করবার দিবাস্বপ্ন দেখত না। Eternal vigilance-এর বদলে দুটো দিনের খুনোখুনি খুব স্পেকটাকুলার বটে, কিন্তু দুটো দিনই তার পরমায়ু।
১৮
সেদিন যে জেনারেল ইলেকশন হয়ে গেল সেটা সম্ভবত ইতিহাসের বিষয়; কিন্তু এত নিঃশব্দে ঘটল যে আমাদের কারুর বিয়েতেও ওর বেশি ধুমধাম হয়। শুনলুম লণ্ডনে না হলেও মফস্সলে বেশ ধুমধাম হয়েছিল। আমাদের নিজস্ব সংবাদদাত্রীর পত্রের কিয়দংশ অনুবাদ করে দিই—‘আমি লেবারকেই ভোট দিলুম, কারণ প্রথমত আমি সোশ্যালিস্ট, দ্বিতীয়ত আমাদের এ অঞ্চলে নির্বাচনটা যাদের নিয়ে তাদের একজনের ছিল যৌবন, মগজ ও উৎসাহ, অন্যজনের জরা, জেদ ও অসামর্থ্য। তবু কিন্তু খুবই আশ্চর্য হলুম শুনে যে, H নির্বাচিত হয়েছেন; কেননা এই অঞ্চলটা সেই থেকেই কনজারভেটিভদের একচেটে হয়ে এসেছে যেদিন নোআ তাঁর আর্ক থেকে বেরিয়ে আসেন। মাত্র গোটা কয়েক ভোটের আধিক্যে H জিতে গেলেন। আমার ঘরের কাছেই একটা নির্বাচনস্থলী। শুক্রবারের রাত্রি পৌনে তিনটের সময় আমার ঘুম ভেঙে যায় যারা ফলাফল জানবার জন্যে অপেক্ষা করছিল তাদের অতি উদ্দাম আনন্দধ্বনি শুনে। যেই আমার চেতনা ফিরল চটি পায়ে দিলুম ও ড্রেসিং গাউন গায়ে দিলুম, আর দৌড়ে গিয়ে ঢুকলুম মায়ের ঘরে—সেখান থেকে রাস্তা দেখা যায়। মাকে বিরক্ত করে জানলা খুললুম, মাথা বাড়িয়ে দিলুম, একজন অচেনা পথিককে জিজ্ঞাসা করলুম, ’কে জিতল? খবরটা শুনে পরম উল্লাসে নিজের ঘরে ফিরে এলুম।’*
মোটের উপর ব্যাপারটা স্বপ্নের মতো লাগল। মাস খানেক আগে এখানে-ওখানে বক্তৃতা চলছিল, ঘরে ঘরে নির্বাচন প্রার্থীদের বিজ্ঞাপন ঝুলছিল এবং কাগজে-কলমে খুবই বাণ বর্ষণ হচ্ছিল। কার কোন পক্ষে ভোট তা একরকম জানাই ছিল, এক ফ্ল্যাপারদের ছাড়া। যে-ই মন্ত্রীদল গঠন করুক জনসাধারণের বড়ো বেশি আসে-যায় না, রাষ্ট্র যেমন চলছিল তেমনি চলে। দোকান-বাজার-থিয়েটার-সিনেমা-ডাকঘর-রেল কোথাও কোনো পরিবর্তন সুস্পষ্ট নয়। আমার ঘরের কাছে যেসব মজুর কাজ করছে তাদের একজন গান ধরেছে। কাবুলিতে গান গায় (‘শ্রীকান্ত’) সেও যেমন অবিশ্বাস্য, ইংরেজেতে গান গায় এও তেমনি অপূর্ব। আমরাই এবার দেশের হর্তাকর্তা, আমাদের র্যামজে সর্দারকে রাজা দেশের সর্দার করেছেন, এই ভেবে তার যদি গান পেয়ে থাকে তবে ধন্য বলতে হবে। নইলে এমন সুন্দর মেঘ ও রৌদ্রের খেলার দিনটাতে কি কেবল পাখিই গান গাইত, মানুষ তার পালটা গাইত না?
ইংরেজ মজুর শ্রেণির লোকেরা খুব শিষ্ট, তারা হল্লা করতে দাঙ্গা করতে শান্তিভঙ্গ করতে জানে না। তবে চিরদিন যে তারা এত সুবোধ বালক ছিল ইতিহাসে কিংবা জনশ্রুতিতে ও-কথা বলে না। ক্রমে ক্রমে ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতির দ্বারা সংঘবদ্ধ হওয়ার পর থেকে ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব স্বীকার করবার পর থেকে তারাই হয়েছে দেশের সবচেয়ে আইন-মানা সম্প্রদায়। আইনের প্রতি অনাস্থা যদি কেউ দেখায় তো সে বড়োলোক, মোটরওয়ালা কিংবা নাইটক্লাবওয়ালি। মোটের উপর ইংরেজ মাত্রেই অত্যন্ত আইন-বশ। পুলিশকে বাধা দেবার কথা তো কেউ ভাবতেই পারে না, পুলিশকে সাহায্য করবার জন্যে সবাই এগিয়ে আসে। এদিকে পুলিশের উপরে খবরের কাগজওয়ালাদের কড়া নজর থাকায় পুলিশও যারপরনাই ভদ্র হয়ে উঠেছে। আগে এতটা ছিল না, তার প্রমাণ আছে। লণ্ডনে গুণ্ডা নেই। ইংল্যাণ্ড দেশটি ছোটো ও সব ক-টি ইংরেজ রক্ত সম্বন্ধে এক হওয়ায় আইন অমান্য করতেও মানুষের সহজে প্রবৃত্তি হয় না, হলেও তেমন মানুষের সঙ্গী জোটে না, ধরা পড়াও তার পক্ষে সোজা। আমার যতদূর অভিজ্ঞতা ইংল্যাণ্ডে ক্রাইম কমে আসছে। দ্বি-বিবাহ ও ভিক্ষুকতা—এ দুটোকে আমাদের দেশে ক্রাইম বলে না, এ দুটোর বিচার করতে এদের আদালতের অনেক সময় যায়। দ্বি-বিবাহ বেশ বাড়ছে বলেই মনে হয়। এ সম্বন্ধে লোকমত হু-হু করে বদলাচ্ছে বলতে হবে। কেননা দ্বি-বিবাহকারীকে বিচারক নামমাত্র সাজা দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছেন এই শর্তে যে, প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ থাকবে না ও প্রথম স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করতে পারবে। যে-দেশে স্ত্রীসংখ্যা পুরুষসংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি সেদেশে এই ব্যবস্থাই সবচেয়ে ভালো। দুয়ো-সুয়ো দুটিকে নিয়ে একসঙ্গে ঘর করাটা নিতান্ত প্রাচ্য প্রথা, তাতে পাশ্চাত্যদের সংস্কারে বাধে।
ইংরেজদের সমাজে আইন যা আমাদের সমাজে আচার তা-ই। অথচ আইন সম্বন্ধে ইংরেজরা প্রতিদিনই বলাবলি করছে যে, ‘অমুক আইনটা এত অযৌক্তিক যে সবাই ওই আইন ভাঙছে, আর পুলিশ নিজেও যখন বোঝে ওটা অযৌক্তিক তখন অপরাধটা দেখেও দেখছে না। এমনি করে একটা আইন ভাঙতে ভাঙতে সব আইন ভাঙতে মানুষ প্রশ্রয় পাচ্ছে। অতএব অমুক আইনটা বদলানো দরকার, তুলে দেওয়া দরকার।’ আচার সম্বন্ধে আমরাও যদি প্রতিদিন এমনই বলাবলি করতুম তবে আচার মাত্রের প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একান্ত ঔদাস্য এবং অশিক্ষিত সাধারণের একান্ত আসক্তি দেখা যেত না। ইংরেজ সমাজের মাথা হচ্ছে ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্ট।* নিকটে যে আমাদের দেশে পার্লামেন্ট-জাতীয় কিছু গড়ে উঠবে ও আমাদের অন্নপ্রাশন থেকে শ্রাদ্ধ পর্যন্ত শাসন করবে এমন আশা করা শক্ত। হিন্দুসভা যদি রাজনৈতিক না হয়ে সামাজিক হয়ে থাকত তবে হয়তো রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি সমাজের পরিকল্পনা তারই মধ্যে মূর্তি পেত। আগে যেমন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি প্রত্যেক জাতের নিজস্ব আচার নিয়ামক সভা ছিল এখন সমগ্র হিন্দুসমাজের তেমনি কোনো সভা কেন হয় না, যে-সভায় প্রত্যেক জাতের প্রতিনিধি বসে সকল জাতের সাধারণ আচার নির্দেশ করবেন? এই সভার অধীনে সামাজিক আদালত থাকে না কেন, যে-আদালতে অনাচারের প্রতিকার হয়? গ্রাম্য স্থবিরদের অত্যাচার থেকে সমাজকে উদ্ধার করে ন্যায়সঙ্গত আচারের প্রতি মানুষকে সশ্রদ্ধ করতে হলে এ ছাড়া অন্য উপায় কী?
ভারতীয় চরিত্রের মূল কথা যেমন সমন্বয়, ইংরেজ চরিত্রের মূল কথা বিনিময়।ইংরেজ কঞ্জুস নয় কিন্তু হিসাবি, একটা পেনিরও হিসাব রাখে; নিজের স্ত্রীর কাছ থেকে নিলে নিজের স্ত্রীকে ফেরত দেয়। আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ হওয়া ইংরেজের পক্ষে অসম্ভব, তার খাদ্য আনতে হয় বিদেশ থেকে, বিদেশকে দিয়ে আসতে হয় পরিধেয় বা অন্য কিছু। এমনি করে তার বিনিময়বোধ পাকা হয়েছে, বণিকসুলভ বৃত্তিগুলি পোক্ত হয়েছে। ফরাসি দোকানদার ও ইংরেজ দোকানদার দুইয়ের তুলনা করলে দেখা যায় ইংরেজ দোকানদার কঞ্জুস নয়, ঠকায়ও না, ভদ্রও; কিন্তু দোকানদারের বেশি নয়, মানুষ নয়। ফরাসি দোকানদার দোষে-গুণে উলটো। ইংরেজকে নেপোলিয়ন দোকানদার বলে সেই যে প্রশংসাপত্রটা দিয়েছিলেন সেটার মর্ম এমন নয় যে ইংরেজ ঠকায়, সেটার মর্ম ইংরেজ বিনিময়শীল। গ্রাহককে খুশি করতে ইংরেজ দোকানদার প্রাণপণ করে, কিন্তু দেনা-পাওনা ভোলে না, আত্মীয়তা করে না। আত্মীয়তার জন্যে ক্লাব আছে, খেলা ক্ষেত্র আছে। দোকানে শুধু প্রয়োজন বিনিময়। আমার ঘরের অনতিদূরে স্বামী-স্ত্রীর দুটো আলাদা দোকান, দুই আলাদা তহবিল, একজনের কাছে আরেক জন সওদা করলে তক্ষুনি বিল লিখে দেয়। এদের দেশে একান্নবর্তী পরিবার কেন গড়ে উঠল না? পরিবারও কেন ভেঙে গেল? যে-কারণে বার্টার থেকে আধুনিক এক্সচেঞ্জ অভিব্যক্ত হয়েছে, সেই কারণে স্বামী-স্ত্রীর দুই উপার্জন দুই তহবিল হয়েছে। সন্তানের জন্যে দু-পক্ষ চাঁদা দেবে, কথা চলছে। তারপর সন্তানরা ঘরকন্নার কাজে সাহায্য করলে মা-বাবার কাছ থেকে মাইনে পাবে এমন কথাও শোনা যায়। এককথায়, যার যতটুকু যোগ্যতা সেটা টাকা দিয়ে পরিমাপ করতে হবে এবং দু-পক্ষের যোগ্যতার ভগ্নাংশ টাকার মধ্যস্থতায় বিনিময় করতে হবে; আমরা ওটা হৃদয়ের মধ্যস্থতায় করে থাকি বলে আমরা এখনও বার্টারের যুগে আছি, আমরা ‘সভ্য’ হয়ে উঠিনি; সভ্যতার লক্ষণ ভগ্নাংশ-ভাগ চুলচেরা বিচার। অতি সূক্ষ্ম ন্যায়। এদেশের ভিক্ষুক যে দেশলাই বেচবার ভান করে পয়সা চায় এও বিনিময়শীলতার বিকার। কিছু না দিয়ে শুধু নিলে পুলিশে ধরে নিয়ে যায়; ওটা একটা ক্রাইম। আইনের চোখে ভিখারি হচ্ছে আসামি!
জগতের অন্তত একটা জাতির এই গুণটি চরিত্রগত হওয়ায় জগতের অনেক ক্ষতি সত্ত্বেও কত লাভ হয়েছে ভাবীকাল তা খতিয়ে দেখবেই। ইংরেজ যতগুলো দেশকে শোষণ ও শাসন করেছে ততগুলো দেশকে এক সূত্রেও বেঁধেছে, ঐক্য দিয়েছে। মৌমাছি যেমন ফুলদের মধু নেয় তেমনি মিলন ঘটায়। মধুটা ঘটকালির মজুরি। তা ছাড়া, মৌমাছিরও তো অন্নদায় আছে। ফুলেরা চাঁদা করে তাকে না খেতে দিলে সে বাঁচে কী করে?
নানা কারণে ইংরেজ এখনও বহুকাল বাঁচবে। প্রথমত, মৌমাছির কাজ এখনও শেষ হয়নি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য একপ্রকার লিগ অব নেশনসই বটে। নতুন লিগ অব নেশনস যতদিন-না শৈশব অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক ঘটকালির দায়িত্ব নেয় ততদিন সে-দায়িত্ব ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ ও ডাচ লিগ অব নেশনসগুলোরই থাকবে। দ্বিতীয়ত, ইংরেজি ভাষা ক্রমশ সার্বভৌম ভাষা হয়ে ওঠায় পৃথিবীর সবাইকেই ইংল্যাণ্ডে এসে ও-ভাষায় নিপুণতা লাভ করে যেতে হবে কিংবা ইংল্যাণ্ড থেকে লোক নিয়ে নিজের দেশে ও-ভাষায় নিপুণতা লাভ করতে হবে। কিছুকাল আগে যখন ফরাসি ছিল বিশ্বভাষা তখন বিশ্ব ছিল ইউরোপ খন্ডের অন্তর্গত। এখন বিশ্বের সীমানা বেড়েছে, এখন কাফ্রির সঙ্গে কাশ্মীরিকে কথা কইতে হবে ইংরেজিতে। Talkies-এর দৌরাত্ম্যে ইংরেজি ভাষার ছিরি যেমনই হোক, প্রচার বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বের ভাষা শিক্ষা-রাজধানী প্যারিস থেকে উঠে এসে লণ্ডনে ও লণ্ডনের চতুষ্পার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত হল বলে। এদিকে কিন্তু বিশ্বের বাণিজ্য-রাজধানী নিউ ইয়র্কে পাড়ি দিল ও যন্ত্রশিল্প-রাজধানী বার্লিন। বার্লিন এখন পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম নগর। তার লোকসংখ্যা বিয়াল্লিশ লাখ। একা বার্লিন শহরেই একশো তেরোটা মাটির উপরের রেলস্টেশন ও একাত্তরটা মাটির নীচের রেলস্টেশন আছে।* এরোপ্লেনের রাস্তা আছে আঠারোটা (গ্রীষ্মকালে), ও সাতটা (শীতকালে)। এখন থেকে প্যারিস হবে কেবলমাত্র আমোদপ্রমোদ রাজধানী এবং জেনেভা রাজনীতি-রাজধানী।
বৃহৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পৃথিবীর সর্বত্র ছড়ানো। এক দেশের অভিজ্ঞতা আরেক দেশে পৌঁছে দেওয়া ব্রিটিশ শাসক সম্প্রদায়ের কাজ। সেই সূত্রে অস্ট্রেলিয়ার অভিজ্ঞতা ভারতবর্ষের কাজে লাগে, ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতা ইজিপ্টের। ইংরেজ জাতিকে বিধাতা ঘরছাড়া করে সৃষ্টি করেছেন, এরা চরে বেড়ায়, খুঁটিতে বাঁধা থেকে জাবর কাটতে জানে না। এই কারণে ইংরেজের সেইসব কোমল বৃত্তিগুলি নেই যা আমাদের আছে, (অনেকটা) ফরাসিদের আছে। কোলের ছেলেকে ভারতবর্ষ থেকে কিংবা হংকং থেকে বিলেতে পাঠিয়ে দেয়। বয়স্ক ছেলের বিয়ের পরে এক শহরে থেকেও কদাচ দেখতে আসে এমন মা-বাবা একমাত্র ইংল্যাণ্ডেই সম্ভব। আমাদের যেমন মামা-মামি মাসি-মেসো কাকা-কাকি ও পিসে-পিসিতে ঘরসংসার জমজমাট, এদের তেমন নয়; গার্হস্থ্য বৃত্তিগুলি এদের ভোঁতা। হৃদয়কে চরিতার্থতা দিলে কাজ নষ্ট হয় যে! বিউটির চেয়ে ডিউটিকে ইংরেজ বড়ো বলে মানে।
অথচ আশ্চর্যের বিষয় প্রেমের কবিতা ইংরেজি ভাষায় যত ও যতরকম এবং যত গভীর অন্য কোনো ভাষায় তত নয়। এক চন্ডীদাস ছাড়া কোনো বাঙালি কবি কোনো দিন সর্বস্ব পণ করে ভালোও বাসেননি, ভালোবাসার কবিতাও লেখেননি। গদ্যকবিদের মধ্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইংরেজিতে প্রেমিক কবির সংখ্যা হয় না। দ্বিতীয়ত, love কথাটার সংজ্ঞা কী তা কোনো ইংরেজ জানে না, তবু বিবাহ করবার আগে love করতে হবে একথা অন্য কোনো সমাজ এতটা জোরের সঙ্গে বলেছে বলে আমার মনে হয় না। আমাদের সমাজে ওটা স্পষ্ট ভাষায় নিষিদ্ধ, আমাদের বিবাহ ব্রহ্মচর্যেরপরে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করবার তোরণ। ধর্মের পরে কাম, তার আগে নয়। ফরাসিরা যদিও প্রেমের নামে গদগদ হয়ে ওঠে ও আমাদের বৈষ্ণব ঠাকুরদের মতো সহস্রবিধ প্রেমের লক্ষণ আওড়ায়, তবু ও-প্রেম মস্তিষ্কজাত (cerebrale) ও বচনবহুল। ওরা মাথা দিয়ে অনুভব করে ও কথা দিয়ে তন্নতন্ন করে; কিন্তু বাণবিদ্ধ কুরঙ্গের বোবা আকুতি ইংরেজরাই বোঝে। Love making ও love এক জিনিস নয়। প্রথমটার চর্চা প্যারিসের একচেটে হতে পারে, কেননা প্যারিসের লোকের হাতে কাজ নেই; দ্বিতীয়টা ইংরেজের মতো অত্যন্ত প্র্যাকটিক্যাল প্রকৃতি কাজের মানুষদের জীবনে অপ্রত্যাশিতরূপে এসে বহু বৎসরের কাজ একদিনে নষ্ট করে দিয়ে যায়।
১৯
ইউরোপের শরৎকাল। পাতাঝরা শুরু হয়ে গেছে। এই তো সেদিন বসন্ত এল সবুজ পাতার পোশাক পরে, যেন কোনো ফ্যান্সি ড্রেসপরা নাচের অতিথি। এরই মধ্যে রঙ্গ শেষ হয়ে এল, বাতি নিবু নিবু, সভা ভাঙে ভাঙে এর পরে পোশাক খুলে ফেলে বিছানায় গা মেলে দিতে হবে। এও এক উদ্যোগপর্ব।
আমাদের দেশে শীতের জন্যে প্রস্তুত হবার কাল হেমন্ত। শরৎ আমাদের দেশে শীতের অগ্রদূত নয়, আমাদের শরৎ স্বাধীন। আমরা শরতের মুখ চেয়ে দিন গুনি; শরৎ আসছে শুনে তার আগমনি গাই; শরৎ চলে গেলে কাঁদি ও কাঁপি। কিন্তু এদের শরৎ যৌবনের শেষের দিকে প্রথম পাকা চুলটির মতো অনাহূত আগন্তুক; আনন্দের নয়, আতঙ্কের পাত্র। এর পিঠ পিঠ শীত আসবেন। তিনি যেমন-তেমন অতিথি নন, স্বয়ং দুর্বাসা। তাঁর অভিশাপে গুটি কয়েক evergreen জাতীয় তরু ছাড়া সকল তরু তরুণীর পত্রসজ্জা নিঃশেষে খসে পড়বে; তারা লজ্জায় কাঠ হয়ে রইবে।
ইংল্যাণ্ড থেকে থুরিঙ্গিয়ায় এসেছি; গ্যেটে শিলার বাখ-এর থুরিঙ্গিয়া, বনরাজিনীলা। অঞ্চলটি বিরলবসতি নয়, গ্রামে গ্রামে কারখানার চিমনি কর্মব্যস্ততার প্রমাণ দিচ্ছে। তবু অঞ্চলটির হাতে অফুরন্ত ছুটি। এতে যেন আকাশের অংশ আছে, আকাশের ব্যাপ্তি। প্রাচীন তপোবন সম্বন্ধে আমার যে-ধারণা আছে তার সঙ্গে থুরিঙ্গিয়ার এই মাটির আকাশটিকে বেশ মানায়। বনের দ্বারা আকাশ ঢাকা পড়বে না, যদি পড়ে তো তপোবনে ও রাজনগরীতে প্রভেদ কোথায়? মানবাত্মার সহজ মুক্তিটিকে রাত্রিদিন উপলব্ধি করবার জন্যেই তপোবন। তপোবনের অত্যাবশ্যক অঙ্গ দশ দিকব্যাপী স্পেস।
থুরিঙ্গিয়ার হাওয়া সমুদ্রবক্ষের হাওয়ার মতো মুক্ত এবং মুক্তির স্বাদে স্বাদু। ইচ্ছা করে সমস্তটা এক নিশ্বাসে শোষণ করি। শহরে থেকে বাতাস আমরা আধপেটা খাই, আমাদের নাসার ক্ষুধা মেটে না। লণ্ডনের মতো শহরে নাক বুজেই থাকতে হয়, অভ্যাসের দোষে পার্কের বাতাসও গ্রহণ করতে প্রবৃত্তি হয় না। স্বয়ং পঞ্চম জর্জেরও সাধ্য নাই যে লণ্ডনের জল হাওয়া বৃষ্টি কুয়াশার অতীত হন। অথচ থুরিঙ্গিয়ার চাষিরাও তাঁর তুলনায় ভাগ্যবান।
গ্যেটের যুগে থুরিঙ্গিয়া আরও বন্য আরও বিজন ছিল সন্দেহ নেই। তাঁর কর্মস্থল ভাইমার এত ছোটো যে প্রায় পল্লিবিশেষ, তখনকার দিনে নিশ্চয়ই ছিল অরণ্যপল্লি। একটি ক্ষীণকায়া স্রোতস্বিনীও আছে তাতে। গ্যেটের দরবারি মনকে অরণ্য সর্বদাই ডাক দিত, তাঁর বাগানবাড়িটি অরণ্যেরই অন্তর্গত একটি কুটির। দরবার থেকে ছুটি নিয়ে সেইখানে তিনি প্রস্থান করতেন। সংসারের প্রাত্যহিক তুচ্ছতার অসংখ্য বন্ধন স্বীকার করেও যে তিনি মুক্তপুরুষ ছিলেন, অন্তত মুমুক্ষু পুরুষ ছিলেন, তার কারণ তিনি কেবল নাগরিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন আরণ্যকও। গ্যেটের মধ্যে আমরা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের যে-সমন্বয়, অন্তত যে-সমন্বয়প্রয়াস দেখি, সে এমনি করেই সম্ভব হয়েছিল। তিনি অ্যারিস্টোক্র্যাট তো ছিলেনই অধিকন্তু প্রকৃতির খুব কাছে কাছে ছিলেন, অন্তত থাকবার জন্যে প্রাণপণ করেছিলেন।* আমি এত বার ‘অন্তত’ কথাটা ব্যবহার করলুম, তার কারণ সকলের মতো আমার ধারণা গ্যেটের ভিতরটায় দু-বেলা কুরুক্ষেত্র চলত—সত্য অসত্যে অষ্টপ্রহর সংগ্রাম। তবু আমার বিশ্বাস তাঁর মধ্যে একটি সহজ সর্বজ্ঞতাও ছিল। তিনি ছিলেন অন্তরে-ঘটতে-থাকা দ্বন্দ্বের অতীত (above the battle)। মহামানবের মতো মহামানবের এই কবিও ছিলেন স্রষ্টাও না বিদ্রোহীও না, নিছক দ্রষ্টা—বিশ্বরূপদ্রষ্টা। গ্যেটের যতগুলি প্রতিকৃতি আমি দেখেছি সেগুলিতে তাঁর চক্ষু আমাকে আকৃষ্ট করেছে তাঁর সকল কিছুর চেয়ে। তাঁর দৃঢ়নিবদ্ধ ওষ্ঠযুগল তাঁর চক্ষুরই বাহন; তাঁর চক্ষুরই সংকল্প তাঁর ওষ্ঠে ব্যক্ত হয়েছে।
‘স্রষ্টাও না বিদ্রোহীও না’—অর্থাৎ তাঁর সত্যকারের যে তিনি, তিনি স্রষ্টাও না বিদ্রোহীও না। তা বলে তাঁর মধ্যে স্রষ্টা ছিল না বিদ্রোহী ছিল না এমন কদাচ নয়। বিশুদ্ধ বিদ্রোহের সুর তো তাঁর সৃষ্টির মর্ম ভেদ করে উঠছে ‘I am the spirit that denies!’ এ বিদ্রোহ অন্নবস্ত্রের জন্যে নয় সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে নয়, এমনকী মুক্তির জন্যেও নয়। বিদ্রোহের জন্যে বিদ্রোহ। উদ্দেশ্য তার সে নিজেই। যেমন, নটরাজের নৃত্য। সাধারণত বিদ্রোহ বলতে আমরা বুঝি সশস্ত্র ভিক্ষুকতা। ভিক্ষা পেলেই বিদ্রোহের ক্ষান্তি। কিন্তু Mephistopheles বলে—
I am the spirit
That evermore deny—and in denying
Everymore am I right—‘No!’ say I, ‘No!’
To all projected or produced—whate’er
Comes into being merits nothing but
Perdition—better then that nothing were
Brought into being—what you men call sin—
Destruction—in short, evil—is my province,
My proper element.
মানুষের মধ্যে এক জন দায়িত্ববান বিধাতা আছেন। আর আছে একজন দায়িত্বহীন অবাধ্য। এই দুজনকে নিয়েই এবং দুজনের অতীত হয়েই মানুষ। এই মানুষের মহানাটক লিখেছেন এমনি মানুষ গ্যেটে।
বিশুদ্ধ দৃষ্টির তপস্যা ভারতবর্ষের পরে এক জার্মানিই করে এসেছে, তাই জার্মানির উপর ভারতবাসীর এত পক্ষপাত। ভারতবর্ষের বাইরে মাত্র একটি ভারতবর্ষ আছে, যেখানে মানুষ ইংরেজের মতো নাগরিক মুক্তিকে কাম্য করেনি, একমনে কামনা করেছে আত্মার মুক্তি। তাই ইংরেজ ফরাসিরা যখন বড়ো বড়ো সাম্রাজ্যের মালিক হল, জার্মানরা তখনও দার্শনিক তর্কে মশগুল এবং সংগীতের সম্মোহনে আবিষ্ট। হোহেনজোলার্নরা জোর করে এদের ধ্যান ভাঙিয়ে দেয়, বিসমার্ক এদের অত্যন্ত কেজো করে তোলেন। আধ্যাত্মিক একাগ্রতাকে বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধির জন্যে প্রয়োগ করে এরা অচিরাৎ এক বিভীষিকা হয়ে উঠল, যেন নৈমিষ্যারণ্যের যোগীরা হঠাৎ ধনুর্বিদ্যা আয়ত্ত করে মৃগয়ায় বাহির হল। গত যুদ্ধে জার্মানির পরাজয় তার মনে লাগেনি, কেননা আসলে ওটা হোহেনজোলার্নদেরই পরাজয়। জার্মানরা স্বভাবত যোদ্ধা নয়, বোদ্ধা। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বিচিত্র দাবি প্রত্যেক জাতিকেই কতকটা স্বভাবভ্রষ্ট হতে বাধ্য করছে—জার্মানিকেও। তাই জার্মানির অতিকৃষ্ট মন যন্ত্রশিল্পের দিকে ধাবিত হয়েছে। যন্ত্রশিল্পে জার্মানির উন্নতি যেমন অদ্ভুত তেমনি কিম্ভূত। ব্রাহ্মণ পন্ডিতের ছেলে গোয়েন্দা পুলিশ হলে যেমন দুর্ধর্ষ হয়ে ওঠে এও তেমনি। এর দয়ামায়া নেই, রুচি-নীতি নেই। বার্লিন শহরটার মতো রাক্ষুসে শহর আমি দেখিনি। মানুষের একটা হাত যদি বাঘের একটা থাবা হয়ে ওঠে তবে ওটাকে ক্রমবিকাশ বলা চলে না। বার্লিনের প্রাণ আছে হৃদয় নেই, রুচি নেই, মাত্রাজ্ঞান নেই।
বার্লিনের পেছনে দীর্ঘকালের ইতিহাস না থাকায় শহরটা কলকাতার মতো অনভিজাত। লণ্ডন-প্যারিস-রোম-ভিয়েনা এমনকী মিউনিখ-ফ্রাঙ্কফুর্ট-ড্রেসডেন-কোলোনের সঙ্গে ওর নাম করতে প্রবৃত্তি হয় না। দ্বিতীয়ত, ওর সঙ্গে মানুষের মহত্ত্বের স্মৃতি জড়িয়ে নেই, জড়িয়ে রয়েছে মানুষের দস্যুতার স্মৃতি। হোহেনজোলার্নরা বুক ফুলিয়ে ডাকাতি করছেন ও তাঁদের শহরটাকে তাঁদের সৈন্যদলের মতো পিটিয়ে মজবুত করছেন। লণ্ডনের নগরবৃদ্ধেরা রাজাদের কাছ থেকে ক্রমাগত নতুন অধিকার আদায় করছেন, ইংল্যাণ্ডের অন্য সর্বত্র যখন যথেচ্ছাচার চলিত ছিল একমাত্র লণ্ডন তখন নিজের নিয়মে নিজে চালিত। প্যারিসও স্বায়ত্তশাসনের দাবি কোনোদিন ছাড়েনি, যদিও সে-দাবি পূর্ণ হয়েছে কদাচিৎ। জার্মানির ‘স্বাধীন নগরগুলো’ লণ্ডন-প্যারিসের মতো বৃহৎ না হলেও মহৎ। কিন্তু বার্লিন ছিল হোহেনজোলার্নদের খাস সম্পত্তি, সবে সেদিন স্বাধীন হয়েই তার একমাত্র অভিলাষ দাঁড়িয়েছে আমেরিকান হয়ে ওঠা।
প্রাশিয়ানদের দেহের মতো মনও বোধ হয় অত্যন্ত ভারী। বার্লিন যেন একখানা রান্নাঘরের শিল, মাটির উপরে এমন চেপে বসেছে যে ভূমিকম্প হয়ে গেলেও নড়বে না। খুব পরিচ্ছন্ন, সুসজ্জিতও বটে, কিন্তু জলদগম্ভীর। বার্লিন থেকে লাইপজিগে এলে মনটা প্রজাপতির মতো লঘুভার হয়ে উড়তে চায়। সংগীতের রাজধানী—সুপ্রাচীন, সুপরিকল্পিত, নাতিবৃহৎ। আধুনিকতার দাবি লাইপজিগও মেনেছে, কিন্তু ইহকালের জন্যেও পূর্বকাল খোয়ায়নি। লাইপজিগ ছাপাখানার রাজধানীও বটে, কিন্তু ছাপাখানার নিনাদ সংগীতকে ও ছাপাখানার কালি নগরসৌষ্ঠবকে ছাপাতে পারেনি।
ড্রেসডেনকে সুন্দর না বলে সুশ্রী বলা ভালো। আমাদের লখনউ-এর সগোত্র। ওর বাস্তুকলায় তেজ নেই, অলংকার আছে। গির্জে এমন হওয়া উচিত যাতে প্রবেশ করামাত্র মন ভক্তিতে ভরে উঠে, অহংকার চোখের জলে গলে যায়, মেরির মাতৃমূর্তি ও যিশুর ক্রুশবিদ্ধ মূর্তি জীবনকে বিষাদমধুর করে। ড্রেসডেনের ফ্রাউয়েন কিরখে তেমন গির্জে নয়। মূর্তি আছে বটে, কিন্তু তাতে মূর্ত হয়েছে শিল্পীর কিংবা শিল্পী যাদের ভৃত্য তাদের বাবুয়ানা। গির্জেতে মানুষের হাঁটু পাতবার কথা, কিন্তু থিয়েটারের মতো আয়েশ করে বসবার আয়োজন করা হয়েছে উপরে-নীচে। ড্রেসডেন কতকটা ভিয়েনার মতো। লাবণ্যকে এরা করে তুলেছে লালিত্য। পথে-ঘাটে ভাস্কর্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, কিন্তু এমনই তার আড়ম্বরপ্রিয়তা যে, কোনো কোনো স্থলে পাথরের উপর সোনার গিলটি করা। ভঙ্গিতেও সরলতার বদলে সর্পিলতা। কিন্তু সর্বত্র একটি লঘুতা সুপরিলক্ষ। প্রাশিয়ার বিপরীত। পাথরের মূর্তি যেন মোমের মূর্তির মতো।
বার্লিন আমাকে হতাশ করেছিল, ড্রেসডেনও করল; ভ্রমণের খাতিরে ভ্রমণ করাতে মোহভঙ্গ নেই, কিন্তু মরীচিকার সন্ধানে ভ্রমণ করা বিড়ম্বনা! কল্পনার আকাশে যা ফোটে মাটির কুসুমে তার আদল কোথায়? মানুষের কল্পনগরী কল্পনাতেই থাকে। তবু কোনো কোনো স্থান আমাকে কল্পনাতীত আনন্দ দিয়েছে। যেমন—প্যারিস, থুরিঙ্গিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া। কল্পনাকে যথাসম্ভব ফাঁকা রেখে বেড়ানো ভালো। তাহলে স্বপ্ন ছুটবে না, স্বপ্ন জুটবে।
কেন ড্রেসডেনকে সুন্দর বলে কল্পনা করেছিলুম? সেখানকার চিত্রশালায় রক্ষিত Sistine Madonna-র প্রতিলিপি দেখে। ফুল সুন্দর হলে ফুলদানিও সুন্দর হবে এমন প্রত্যাশা স্বাভাবিক; নইলে যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের যোজনা হয় না—বাস্তবে যা-ই হোক আদর্শে অসংগতি আসে। ভেবেছিলুম ওই একখানি ছবি যে-সৌন্দর্য বিকীরণ করছে তাই দিয়ে ড্রেসডেন সুন্দর হয়ে গেছে। তা হয়নি। তবু সুখদৃশ্য হয়েছে, সেই অনেক।
Sistine Madonna-কে প্রত্যক্ষ করে ধন্য হয়েছি। বুঝেছি, মানুষ বংশানুক্রমে মরবে, কিন্তু এমন আনন্দকে মরতে দেবে না। রাজা গেছেন রিপাবলিক এসেছে, সেও যাবে, কমিউন আসবে। কিন্তু যৌতুকরূপে যে নিধি একদিন ইটালি থেকে ড্রেসডেনে এসেছিল, পৃথিবীসুদ্ধ মানুষ তাকে বাঁচিয়ে রাখবেই। রাফেল মানুষের দেশে সাঁইত্রিশ বছর মাত্র ছিলেন। তাঁর চেয়ে দীর্ঘজীবী লক্ষ লক্ষ ছিল ও আছে, কিন্তু সকলে যাকে মরলেও মরতে দেয় না সেই ভাগ্যবান অমর।
তুলি ও রং দিয়ে পটের উপর রক্ত-মাংসের মানুষ সৃষ্টি করতে বিধাতাও পারতেন না। গতিহিল্লোলময়ী ম্যাডোনার বসনের খস খস শুনতে পেলুম। শিশু যিশুর সর্বাঙ্গের চপলতা চাউনিতে একীকৃত হয়েছে। তরুণী মা তাঁর দুরন্ত শিশুকে কোল থেকে নামতে দিচ্ছেন না, তাঁর চাউনিতে ভয়। দেবতা এখানে প্রিয় হয়েছেন, মানুষ হয়েছেন।
ড্রেসডেন থেকে এলবে নদী ধরে প্রাগ যাবার পথটি অতুলনীয়। নদীর বাঁধ যেন উঁচু হতে হতে পাহাড় হয়ে গেছে, তাও দেওয়ালের মতো খাড়া। চেকোস্লোভাকিয়া ওরফে বোহেমিয়া পর্বত-বন্ধুর, যদিও প্রাগ অঞ্চলটি সমতল। প্রাগ নিজে বন্ধুর ও পাষাণ-পিহিত। প্রাগের বিশেষত্ব, প্রাগ প্রাচীন অথচ অত্যন্ত নবীন। কলকারখানাতে ও সুপরিপাটি বস্তিতে এর প্রাচীন অংশটি ঢাকা পড়ে গেছে। রাজপথের ভিড় ঠেলে (প্রাগের লোকসংখ্যা বহুগুণ বেড়ে গেছে স্বাধীনতার পর থেকে) পুরাতন শহরের খানিকটা দেখা যায়, কিন্তু প্রাগ যেমন কালের সঙ্গে তাল রেখে ছুটেছে মনে হয় অচিরেই আমেরিকান কলেবর ধারণ করবে।
চেকরা দীর্ঘকাল নাবালক থাকার পর এই সেদিন আত্মপ্রকাশের অবকাশ পেয়েছে, উৎসাহ তাদের তরুণ বয়সের অরুণ আভার মতো দিগদিগন্ত উৎসর্পী। অন্যান্য দেশের কোনোটাতে জেতার মোহভঙ্গ, কোনোটাতে পরাজিতের গ্লানি, কিন্তু চেকোস্লোভাকিয়ায় ঊর্ধ্বপ্লাবী নির্ঝরের মতো আকাশের সঙ্গে কুস্তি করবার আগ্রহ। (চেকদের এরোপ্লেন সংখ্যা অনুপাত-অতিরিক্ত)। বোহেমিয়া দেশটি পুরাতন হলেও চেকরা নতুন জাতি, তাদের অতীত বড়ো নয় বলে তাদের ভবিষ্যতের উপর মন। এই কয়েক বছরে তারা বৈষয়িক উন্নতি তো করেছেই, শিক্ষাদীক্ষায় ইউরোপকে নতুন আদর্শ দিয়েছে, নতুন সম্ভাবনা দেখিয়েছে এবং সংগীতে তাদের এত একাগ্রতা দেখে মনে হয় নিকট ভবিষ্যতে তাদের ভিতর থেকেই ইউরোপের গুণীদের আবির্ভাব হবে।
চেকদের রক্ত নতুন, সেটা তাদের প্রথম সুবিধা। চেকদের মনের জমিতে অস্ট্রিয়ান-জার্মানরা ভাবের পলিমাটি বিছিয়ে দিয়ে গেছে, সেটা তাদের পরম সুবিধা। আমরা ইংরেজদের কাছ থেকে দ্বিতীয়টা পেয়েছি, অথচ নিজেদের কাছ থেকে প্রথমটা পাইনি বলেই ভাবনা। এর প্রতিকার বর্ণ-সাংকর্যের দ্বারা রক্তকে নতুন করা। সভ্যতার প্রাচীনতা ভালো জিনিস, কিন্তু রক্তের প্রাচীনতা মারাত্মক। রক্তকৌলীন্যের মোহে যে জাত মজেছে, তার সভ্যতাও মিউজিয়ামের মমি হয়ে গেছে। ভারতের স্বাধীনতার চেয়ে ভারতের নবীনতা আরও জরুরি। আমাদের অতীতের চেয়ে আমাদের ভবিষ্যৎকে যেদিন দীর্ঘতর বোধ হবে সেইদিন আমাদের নিশান্ত হবে, আমরা প্রভাতের চাঞ্চল্য সর্বাঙ্গে অনুভব করব। স্বাধীনতার বিপুল দায়িত্ব বইবার প্রসন্ন ধৈর্য সেই চাঞ্চল্যের আনুষঙ্গিক।
নুর্নবার্গ সুন্দর। কিন্তু নুর্নবার্গ একটি নয়, নুর্নবার্গ দুটি। পুরাতন নুর্নবার্গের সীমানার বাইরে নতুন নুর্নবার্গ তার অসংখ্য কারখানায় স্টিম ইঞ্জিন, মোটর গাড়ি, খেলার পুতুল তৈরি করছে। পুরাতন নুর্নবার্গ তার স্বকীয়তা রক্ষা করে পৃথিবীর চারুশিল্পমোদীদের তীর্থস্থলী হয়েছে। প্রাচীন রীতির বাস্তুগুলি তেমনি আছে। ভ্রম হয় এ কোন শতাব্দীতে এসে পড়লুম! দুর্গপ্রাচীর, তোরণ, গম্বুজ, পরিখা বিংশ শতাব্দীর বাস্তবের মাঝখানে মধ্যযুগের স্বপ্নকে ধরে রেখেছে, মধ্যরাত্রির স্বপ্নের জের মধ্য দিবায় চলেছে।
নুর্নবার্গ যেদিক দিয়ে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে সেটা চারুশিল্পের নয়, যন্ত্রশিল্পের দিক। জার্মানিতে দেখা গেল যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের কেবল যে প্রয়োজনসিদ্ধির সম্বন্ধ আছে সেকথা সত্য নয়, যন্ত্রের প্রতি মানুষের গভীর মমতা আছে। জার্মানিতে যন্ত্রকে মানুষ ততখানি ভালোবেসে সেবা করে ইংল্যাণ্ডে ঘোড়াকে যতখানি, কিংবা ভারতবর্ষে গোরুকে যতখানি। বার্লিনের লোক যেন যন্ত্রের আত্মাকে দেখতে পেয়েছে, যন্ত্র যেন তাদের কাছে যন্ত্র নয়, আত্মীয়। আধুনিক যুগে যন্ত্র যেসব সমস্যার সূত্রপাত করেছে তাতে যন্ত্রের প্রতি রাগ হবারই কথা। কিন্তু ও যে মানুষের আত্মজ। পুত্র কি পিতা-মাতাকে কম জ্বালাতন করে?
হল্যাণ্ড আমাকে অবাক করেছে। দেশটি আমাদের যে কোনো একটা বড়ো জেলার চেয়ে বড়ো নয়। তবু তার সাম্রাজ্য আছে তার থেকে বহু সহস্র ক্রোশ দূরে। তার চেয়েও যা বড়ো কৃতিত্ব—হল্যাণ্ড সমুদ্রকে পিছু হটাতে লেগেছে। সমুদ্র হল্যাণ্ডের বেগার খেটে দিয়ে আসছে কবে থেকে। তার খালে জল ভরে দেয়, খেতে জলসেচ করে, তার অসংখ্য জাহাজকে পান্ডার মতো পৃথিবী পরিক্রমায় নিয়ে যায়। ইংরেজ সমুদ্রের কাছ থেকে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমি আদায় করতে পারেনি, ওলন্দাজ তার বেশিরভাগ ভূমি সমুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করে কেড়ে নিয়েছে।
হল্যাণ্ড এখন বিশ্বজনের শান্তিপঞ্চায়েতকে চন্ডীমন্ডপ ছেড়ে দিয়েছে। The Hague শুধু হল্যাণ্ডের রাজধানী নয়, আন্তর্জাতিক রাজধানীগুলোর অন্যতম। আমি যে-সময় জেগে ছিলুম সে-সময় ফরাসি-ইটালিয়ান-বেলজিয়ান প্রতিনিধিদের সঙ্গে ফিলিপ স্নোডেনের বচসা চলছিল। হোটেলগুলোতে নানা নেশনের পতাকা উড়ছিল, সমুদ্রের কূলে লোকারণ্য। কত দেশের লোক! সমুদ্রকূলে স্ত্রীস্বাধীনতার মাত্রাটা কিছু বেশি হয়েই থাকে।
বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস যেন প্যারিসের শহরতলি। ব্রাসেলসের যেটুকু প্রাচীন সেইটুকু তার বিশেষত্ব। যেমন তার গির্জে এবং টাউন হল (Hotel de ville) প্রাচীন জার্মানিতে প্রতি নগরেই রাট হাউস ছিল, এগুলি সার্বজনীন ক্রিয়াকর্ম আমোদ-আহ্লাদ আহার-বিহারের কেন্দ্র। ইংল্যাণ্ডের টাউন হলগুলিতে নাচ-গান হয়। আমরা টাউন হল করেছি, কিন্তু বক্তৃতার জন্যে। আমাদের নগরগুলি কেন্দ্রহীন।
২০
অক্টোবর মাসের প্রারম্ভে যখন ইংল্যাণ্ডের আকাশে বাতি নিবিয়ে দিয়েছে, অষ্টপ্রহর বৃষ্টি ও বৃষ্টির আনুষঙ্গিক শীত, তখনও ইটালির অকাশ নীল নির্মেঘ সূর্যকরোজ্জ্বল। বনে বনে তখনও পাতাঝরার দেরি। ছায়াতরুতলে রৌদ্র সন্ত্রস্তা ধরণীকে তখনও আশ্রয়ভিক্ষা করতে হয়।
ইটালি যেন আমাদের দেশ। সূর্য যে যে দেশের প্রতি সদয় তাদের মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতিগত মিল আছে। গাছপালার মতো মানুষও বেঁটেখাটো এবং প্রভূতসংখ্যক। নারীর মুখে সুকুমার কমনীয়তা এবং বেশে ও কেশে সেকেলে রীতি। ভিক্ষুক ও সন্ন্যাসী ভগবানের মতো সর্বত্র অবস্থিত। চর ও চোর পবনের মতো অদৃশ্যবিহারী। মানুষের মতো ও মদের মতো মাটিও রঙিন মেঘও রঙিন। কোথাও স্রোতোবেগহীন নীল সলিল হ্রদের অঙ্কে সৌধশোভিত বিলাসদ্বীপ, হ্রদকে প্রায় বেষ্টন করেছে আল্পস পর্বতের শাখাপ্রশাখা। কোথাও দিগন্তপ্রসারী সমতল শস্যক্ষেত্র, তিন হাজার বছরের পুরাতন জমি, তার উপর দিয়ে কত যুগ-যুগান্তরের সৈনিক জয়যাত্রায় গেছে ও তার নীচে কত নগরী প্রোথিত হয়েছে। কোথাও ভগ্ন ক্রীড়াস্থলী, ভগ্নবিশিষ্ট স্নানাগার, ভাঙা মঠ, ভাঙা গির্জা। রাশি রাশি স্মৃতিচিহ্ন স্মৃতিকে ভারাক্রান্ত করছে! মানুষ তিন হাজার বছরের পাষাণময় চিৎকারে কর্ণক্ষেপ না করে একটা দু-দিনের পুরোনো হালকা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে কাজ করছে। লক্ষ লক্ষ প্রস্তরমূর্তি দেশটাকে যেন মিউজিয়ামে পরিণত করতে চায়, কিন্তু দেশ তাদের প্রতি দৃকপাত করছে না, বিদেশিরা করছে।
ভারতবর্ষের সঙ্গে ইটালির ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক সাদৃশ্য সকলেই লক্ষ করেছেন। আজকের ইটালি দেখলে কালকের ভারতবর্ষ দেখা হয়। ইটালি যথাসম্ভব তার স্বধর্মের অনুসরণ করছে। সে যে ইংল্যাণ্ড নয় ইটালি একথা যদি পদে পদে মনে রাখি তবে ইংরেজের চোখে ইটালি দেখার মতো ভুল দেখা ও ইংরেজের অভিজ্ঞতা দিয়ে ইটালিকে বিচার করার মতো ভুল বিচার ঘটে না। ফ্যাসিস্ট সংঘ রোমান ক্যাথলিক চার্চের বংশে জন্মেছে এবং রোমান ক্যাথলিক চার্চ রোমক সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী। একচ্ছত্র অধিনায়কের আজ্ঞাধীন অক্ষৌহিণী ইটালিতে নূতন নয়। সমষ্টির মধ্যে ব্যষ্টিকে বিলীন করা ইটালীয়-র চিরাভ্যাস। চার্চ যদি বহির্মুখীন না হত তবে ইটালি গত সহস্র বৎসরে বহুধাবিভক্ত হত না এবং আজ তার বিলম্বিত প্রতিকারস্বরূপ ফ্যাসিস্ট সংঘ প্রতিষ্ঠা করত না।
তা করুক, কিন্তু নিজের ঘরের বাইরে পরের ঘরে পদক্ষেপ করতে চায় কেন? বিশ্বসুদ্ধ সবাই ফ্যাসিস্ট হতে যাবে কোন দুঃখে?
এর উত্তর, ইটালীয় চরিত্র বাঙালি চরিত্রের মতো কল্পনাকে খাটো করলে বল পায় না। মারি তো গন্ডার, লুটি তো ভান্ডার। কিন্তু বাঙালি চরিত্রে যা নেই কিংবা অল্প আছে, ইটালীয় চরিত্রে সেই অভিনয়শীলতা বিদ্যমান। ইটালীয়রা অভিনয়ের পোশাক পরে অভিনয়ের ভঙ্গিতে কথা বলতে ভালোবাসে। তাদের চুল ছাঁটা ও টেরি কাটা, তাদের জুলপি ও ভুরু অভিনয়ের মেক আপ। তাদের মুখের মাত্রাহীন অত্যুক্তি তাদের নিজেদের কানে সুধাবর্ষণ ও প্রাণে আত্মপ্রসাদ বিতরণ করে। সত্যিই তারা জগৎ গ্রাসিতে আশয় করেনি, যদি-বা করে থাকে তবে ও-জিনিস তাদের ক্ষমতায় কুলাবে না এ তারা মর্মে মর্মে জানে। তবুও কথা থিয়েটারি ঢঙে না বলতে পারলে তারা নিজেদেরকে কাপুরুষ জ্ঞান করে।
বাষ্প থেকে জল হয়, জল থেকে হয় বরফ। বরফের অবয়বে বাষ্পের আদল খুঁজলে নিরাশ হতে হয়। তেমনি আধুনিক ইটালীয়ের চরিত্রে রোমক চরিত্রের আদল। সে-ওজস নেই, সে-ঋজুতা শুধু ইটালীয় চরিত্র থেকে কেন, সভ্য মানবচরিত্র থেকে গেছে, এবং সেই শাসনকৌশল ইংরেজ চরিত্র আশ্রয় করেছে। কিন্তু ততঃ কিম? মাতসিনি, গ্যারিবল্ডি, ক্রোচে ও দুজে (Duse)-র জাতিও নানা গুণে ভূষিত। একটি বৃহৎ আদর্শবাদ ইটালীয় চরিত্রের কোথাও উহ্য আছে। তারই বলে ধীরে ধীরে ইটালি জগৎসভায় আসন করে নিচ্ছে, কিন্তু এতটা ঢক্কানিনাদ সহকারে যে কান জানে ঢক্কাই সত্য।
যে-ইটালি পৃথিবীর সকল দেশের মধ্যে সৌন্দর্যস্রষ্টারূপে শ্রেষ্ঠ এবং অমর, সে-ইটালি রোমক যুগের নয় আধুনিক যুগের নয়; সে-ইটালি দান্তে পেত্রার্কা লেওনার্দো মিকেলাঞ্জেলোর মায়াময় যুগের, যে-যুগে রোমান্স ছিল মানুষের জীবনবস্তু। শেক্সপিয়ারের নাটকে ও ব্রাউনিঙের কাব্যে আমরা তার আলেখ্য দেখছি। একই মানুষ পাথর কেটে মূর্তি গড়ছে, প্রাচীরগাত্রে ছবি আঁকছে, শব ব্যবচ্ছেদ করে শরীরতত্ত্ব চর্চা করছে, নগররক্ষী সৈন্যের নায়ক হচ্ছে, নির্বাসিত হয়ে নানা সংকটের আবর্তে পড়ছে। ‘জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন।’ এদের প্রেমকাহিনি যেমন বিচিত্র তেমনি বীরত্বপূর্ণ তথা করুণ। আমাদের যুগে সৌন্দর্যসৃষ্টির স্রোত আবর্জনায় মন্থর, নানা কুটিল থিয়োরির কচকচি শিল্পীর স্বতঃস্ফূর্তিকে ব্যাহত করছে। মধ্যযুগের সহৃদয়তার পরিবর্তে আধুনিক যুগের সমস্তিষ্কতা হয়েছে শিল্পসৃষ্টির কষ্টিপাথর। মধ্যযুগে সর্বাঙ্গীণ ব্যক্তিত্ব ছিল শিল্পী মাত্রের কাম্য, আমাদের যুগের শিল্পী কেবলমাত্র শিল্পী হয়েই ক্ষান্ত। সেইজন্যে শিল্পে জীবনের সবটার ছাপ পড়ছে না, জীবনের সুগোল সুডৌল রূপটি শিল্পের খর্বক্ষীণ আলিঙ্গনে আঁটছে না।
মধ্যযুগের ইটালি ধর্মপ্রাণও ছিল। তার সাক্ষী ভারতবর্ষের মতো ইটালির সর্বঘটে। কিন্তু এই ধর্মপ্রাণতা কেমন সংকীর্ণ ছিল তার একটি নমুনা রোমে পাওয়া যায়। রোমক যুগের সরল উন্নত নিরীশ্বর মন্দিরগুলিকে ভেঙে তাদের থেকে পাথর খুলে নিয়ে ক্যাথিড্রাল নির্মাণ করা হয়। সেসব ক্যাথিড্রাল যদি সুন্দর হত তবে এই অপরাধের মার্জনা থাকত, কিন্তু রোমের দুটি-একটিকে বাদ দিলে বাকি সমস্ত গির্জা জাঁকজমকের জোরে দর্শককে পীড়ন করে এবং লক্ষ লক্ষ ধর্মভীরু তীর্থযাত্রীর মনে সম্ভ্রম জাগায়। ফ্লোরেন্সের ক্যাথিড্রাল তস্করের নয়, শিল্পীর কীর্তি। মিলানের ক্যাথিড্রাল বিরাট গম্ভীর বহু শীর্ষ বহু মুখ। ভেনিসের ক্যাথিড্রাল সাড়ম্বর প্রাচ্য প্রভাবসম্পন্ন।
ভেনিসের গৌরবের দিনে ভেনিস ভাবীকালের জন্যে এমন কিছু রেখে যায়নি যার জন্যে ভাবীকাল তার প্রতি সশ্রদ্ধ হতে পারে। তবে ভেনিস নিজেকে দিয়ে গেছে, সে-দান সামান্য নয়। সমুদ্রের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে সেই মাটির উপর ভেনিসের প্রতিষ্ঠা, তার পিছনে সাধনা ছিল এবং সাধনার সম্মান করতে হয়। চন্দ্রালোকিত ভেনিসের খালে খালে গন্দোলায় আন্দোলিত হয়ে আনন্দ আছে, কিন্তু দুর্গন্ধের ভয়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে। ভেনিসের যৌবনকালে ভেনিস কেমন রঙ্গিণী ছিল অনুমান করতে পারি সুসজ্জিত গন্দোলায় নৃত্যগীতের আয়োজন থেকে ও গন্দোলার সঙ্গে গন্দোলার গতি প্রতিযোগিতা থেকে। গন্দোলায় করে এক বাড়ির থেকে আরেক বাড়িতে ও এক পাড়া থেকে আরেক পাড়ায় যাওয়ার মোহ উপেক্ষা করা যায় না। কিন্তু সম্প্রতি কলের গন্দোলা দেখা দিয়েছে। সে-গন্দোলার চলায় ছন্দ নেই, ধীরতা নেই, গাম্ভীর্য নেই। ভেনিসের গন্দোলিয়েররা খাসা মানুষ। তাদের পেশা ও প্রকৃতি বদলালে ভেনিসের অঙ্গহানি ঘটবে। কিন্তু যে-নগরী মৃতা তার অঙ্গহানি ঘটলেই-বা কী, না ঘটলেই-বা কী!
ফ্লোরেন্স এখনও বেঁচে। এখনও সেখানে ও তার অনতিদূরে জীবন্ত শিল্পীরা বাস করে; কিন্তু মৃত শিল্পীদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় কি? কতকটা তাদের নকল ও বাকিটা তাদের শ্রাদ্ধ করে। ফ্লোরেন্সের মাটির উপরে সৌন্দর্যের খনি। এককালে এ নগরী কেমন ‘পুষ্পিতা’ ছিল, কল্পনা করেও আনন্দ, আবার তার এত কিছু স্মারক রয়েছে যে প্রত্যক্ষ করেও আনন্দ। পাছে জার্মানরা লুঠ করে নিয়ে যায় সেই ভয়ে মহাযুদ্ধের সময় ফরাসিরা প্যারিস থেকে মোনালিসা ও ভিনাস ডি মাইলোকে দক্ষিণ ফ্রান্সে সরিয়ে ফেলে। কিন্তু শত্রু যদি ফ্লোরেন্স আক্রমণ করে তবে তার আগে ফ্লোরেন্সের কয় সহস্র শিল্পসৃষ্টি সরানো সম্ভব হবে? বোধ করি তাই ভেবে সেকালের শিল্পীরা ফ্লোরেন্স রক্ষার জন্যে অস্ত্রহস্তে দুর্গপ্রাচীরে দাঁড়াত।
রোমকে কেন Eternal City বলে তার অর্থ বুঝি যখন জানি কুলাম পাহাড়ের পিঠে দাঁড়িয়ে রোমের ভিতর ও বাহির পরিক্রমা করি। অনেকগুলি পাহাড় পাহারা দিচ্ছে। কম নয়, তিন হাজার বছরব্যাপী পাহারা। কত দিগবিজয়ের সংবাদ নিয়ে দূত এসেছে, তার পরে বীর এসেছে, নগরী উৎসব-প্রমত্তা ও বিনিদ্রা হয়ে তার পায়ে লুটিয়ে পড়েছে, এই প্রহরীদের স্মরণে সেসব যেন সেদিনের কথা। একদিন বিজেতারা কতগুলি খ্রিস্টান দাস নিয়ে এল। দাসদের ধর্মকে উপহাস করল। বাঘ-সিংহদের সামনে দাসদের ছেড়ে দিয়ে তাদের মরণ-তামাশা দেখল। ক্রমে একদিন সম্রাট হলেন খ্রিস্টান, রাষ্ট্র হল খ্রিস্টান, রাজগুরুই হলেন রোমের মালিক। রোমকে কেন্দ্র করে তাঁর দূতেরা ইউরোপের সকল রাজ্যে চারিয়ে গেল, প্রথমে রাজন্যদের ও পরে প্রজাদের দীক্ষা দিল। এবার রোমের পর্বত প্রহরীরা দেখল আরেকরকম দিগবিজয়ের উৎসব। রোমের পোপ হলেন খ্রিস্টীয় জগতের পিতা। এককালে যেমন উচ্চাভিলাষীরা সিজার হওয়ার জন্যে তপস্যা ও চক্রান্ত করত, আরেক কালে তেমনি পোপ হওয়ার জন্যে উঠেপড়ে লাগল। ইউরোপ উজাড় করে যাত্রীরা চলল রোমের অভিমুখে। তাদের জন্যে ক্যাথিড্রাল খাড়া হল, সহস্র সহস্র যুবক সন্ন্যাসী হয়ে গেল। তাদের জন্যে মঠ তৈরি হল। দাসদের যাজক প্রাসাদবাসী হয়ে বিস্তীর্ণ জমিদারির ওপর রাজাগিরিও করলেন। ভাটিকানো অলংকরণ করতে বড়ো বড়ো শিল্পীরা নিমন্ত্রিত হয়ে এল। রোমের প্রহরীরা আরেকরকম দিগবিজয়ীর সাক্ষাৎ পেয়ে ধন্যহল।
পোপ যখন থেকে কেবলমাত্র ইটালির না হয়ে খ্রিস্টীয় জগতের হলেন তখন থেকে ইটালির আত্মা প্রতিভূ হারিয়ে রোমের বাইরে ছোটো ছোটো নগরে ও প্রদেশে প্রতিনিধি খুঁজতে ও পেতে থাকল। যে ইটালি ধ্যানী ও প্রেমিকদের মনে আইডিয়ারূপে ছিল, নেপোলিয়নের নিষ্ঠুর হস্ত ও কাভুরের চতুর মস্তিষ্ক তাকে মূর্তিমতী করল। মুসোলিনির কান্ড দেখে সন্দেহ হচ্ছে সে-মূর্তি শিবানী না বানরী, কিন্তু মাতসিনির মানসী চিরকাল ভাবলোকে থাকবেন না, ভাবীকালের আদর্শবাদী এই অসম্পূর্ণ মূর্তিকে নিজের হাতের বাটালি দিয়ে কুঁদে তার মধ্যে সেই মানসীকে অবতরণ করাবে।
২১
ইউরোপ থেকে বিদায়ের দিন নিকট হয়ে এল। দীর্ঘ দুই বছর পরে আমার বিরহী বন্ধুটি তার সুখনীড়ে ফিরছে। ইউরোপ ছিল তার নির্বাসনভূমি। তাই বিদায় দিনটি তার মুক্তির দিন। কিন্তু আমার?
ইউরোপকে আমি না দেখেই ভালোবেসেছিলুম, দেখেও ভালোবাসলুম। ইউরোপ আমাকে চিরকাল আকর্ষণ করে এসেছে—অন্য কথায়, চিরকাল ভালোবেসে এসেছে। ইউরোপ থেকে বিদায় আমার পক্ষে বিরহের শেষ নয়, শুরু।
তাই কখনো চোখের পাতা আদ্র হয়, কখনো বুকের কাঁপন তীব্র হয়। মনটা বিশ্বাস করতে চায় না যে বিদায়ের দিন সত্যিই আসবে—‘একদিন এই দেখা হয়ে যাবে শেষ।’ বিদায়ের ভাবনা যথাসাধ্য ভুলে থাকলুম। তবু যখনই মনে পড়ে যায় তখনই আমার ইটালিবিহার করুণ হয়ে ওঠে। আহা, আবার কবে দেখব—যদি বেঁচে থাকি, যদি পাথেয় জোটে, যদি এই ভালোবাসা এমনই থাকে! এতগুলো যদির উপর হাত চলে না গো ইউরোপা। মানুষের সঙ্গে ভালোবাসা ও দেশের সঙ্গে ভালোবাসা এ দুইয়ের মধ্যে একটু তফাত আছে। তুমি যেখানে থাকলে সেইখানেই থাকলে। মানবী হলে নিশ্চয়ই আমার দেশে আমার সঙ্গে দেখা করতে যেতে। তা যখন তুমি পারবে না তখন আমাকেই আসতে হয়। অন্তত বলতে হয় যে আবার আসব।
বললুম, আবার আসব, ভয় কী? কতই-বা দূর! জলপথে পনেরো দিন, স্থলপথে বারো দিন, আকাশপথে সাত দিন মাত্র। কিছু না হোক, মনের পথে একমুহূর্ত।
বললুম ও-কথা। তবু জানতুম ও-কথা মিথ্যা। জীবনে ফিরে আসা যায় না। এক বার মাত্র আসা যায় এবং সেই আসাই শেষ আসা। আবার যদি আসি তবে দেখব সে-ইউরোপ নেই। সেই পুরাতন পদচিহ্ন ধরে মার্সেলস থেকে প্যারিস, প্যারিস থেকে লণ্ডন যাব। লণ্ডনের গলিতে গলিতে বেড়াব। ইংল্যাণ্ড থেকে ফ্রান্সে ও সুইটজারল্যাণ্ডে, জার্মানিতে ও অস্ট্রিয়ায়, হাঙ্গেরিতে ও চেকোস্লোভাকিয়ায় স্মৃতির দাগে দাগা বুলাব। ইটালি প্রদক্ষিণ করে চেনা জিনিসগুলিকে খুঁজে বের করব। দুটি বছর কাটবে দুটি বছরের পুনরাবৃত্তি করতে। চাইনে নতুন দেখতে, নতুন করে দেখতে। আমার তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সের এই আমি আমার শ্রেষ্ঠ আমি। এই দুটি বছরে যা পেলুম তার বেশি এ জীবনে পাওয়া যাবে না। এই-বা কজন পায়? এত জ্ঞান, এত মান, এত প্রীতি, এত মমতা! চক্ষু যত দেখল লেখনী তার ভাষা পায়নি, আভাস দেবার সাধনা করেছে। শ্রবণ যত শুনল স্মরণ রাখতে পারল না।
স্মৃতির দাগ আপনি মুছে যায়। স্মৃতির পথ বেয়ে কত পথিকের আনাগোনা, তাদের চরণতল মৃত্যুর মতো নির্দয়। তবু যদি স্মৃতির দাগ ধরে যাওয়া সম্ভব হয় তবে কোন ইউরোপকে দেখব? ইউরোপ তো শুধু স্থান নয়, দৃশ্য নয়, সে মানুষ—ইউরোপের মানুষ। সেই মানুষগুলি কি আমার অপেক্ষায় অপরিবর্তিত রূপ নিয়ে অচঞ্চলভাবে আমার স্মৃতিনির্দিষ্ট স্থানে কেউ-বা বসে, কেউ-বা দাঁড়িয়ে, কেউ-বা টমটম হাঁকিয়ে, কেউ-বা ঠেলাগাড়ি ঠেলে, কেউ-বা বইয়ের উপর ঝুঁকে রয়েছে?
পদে পদে পরিবর্তনশীল ইউরোপ। ততোধিক পরিবর্তনশীল মানুষের জীবন-যৌবন জীবিকা ও প্রেম। স্মৃতিতে যাদের যে-সময়ের যে-অবস্থার ফোটো রইল তারা যদি-বা জীবিত থাকে তবু তাদের সে-বয়স আর থাকবে না। তাদের মধ্যে যারা আকস্মিকভাবে আমার দৃষ্টিপথে পড়েছিল, তাদের নাম ঠিকানা আমি হাজার মাথা খুঁড়লেও পাব না। রাইন নদী চিরকাল থাকবে, স্টিমারও তাতে চলতে থাকবে। কিন্তু সেই যে মেয়েটি তরুণী ও সুন্দরী হয়েও মুখে রং মেখেছিল তাকে তার প্রেমিকের স্কন্ধলগ্নরূপে আর একটিবার দেখতে পাব কি? না যদি পাই তবে রাইনের উভয়তটের গিরিদুর্গ তেমন সুদৃশ্য বোধ হবে না। লোরলাইয়ের মায়া সংগীত শুনে নাবিকরা যেখানে প্রাণ দিত সেখানে আমার বুকের স্পন্দন হঠাৎ স্থির ও তার পরে প্রবল হয়ে উঠবে না।
এমনি কত দৃশ্য অঙ্গহীন মনে হবে। সেই জন্যে কি মার্সেল প্রুস্ত বহির্জগতের প্রতি অন্ধ ও বধির হয়ে ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে স্বেচ্ছা বন্দিরূপে অবস্থান করতেন? আমাকেও তাহলে শপথ করতে হয় যে আর ইউরোপে আসব না, পাছে প্রিয়ববরাকে অঙ্গহীনা দেখি, পাছে পরিচিতাকে অপরিচিতা বলে ভুল হয়। সে ভুলের সংশোধন নেই। বিরহের পরে প্রত্যেক প্রেমিককে ভয়ে ভয়ে প্রিয়ার দিকে চাইতে হয়—সে মোটা বা রোগা হয়ে যায়নি তো; অপরে তার মন চুরি করেনি তো? নানা অভিজ্ঞতার চাপে পূর্বস্মৃতি কি তার মনে কিছুমাত্র অবশিষ্ট আছে?
একদিন ঘুম থেকে জেগে দেখলুম চারিদিকে সমুদ্র। সমুদ্রের একটিমাত্র পরিচয় সে সমুদ্র। সে যে ভূমধ্যসাগর, ও কথা তার গায়ে লেখা নেই। চীনের সাগরও হতে পারে, অস্ট্রেলিয়ার সাগরও হতে পারে।
মাটি যে আমাদের কত বড়ো আশ্রয়স্থল সমুদ্রের উপর অসহায়ভাবে ভাসমান না হলে হৃদয়ংগম হয় না। সমুদ্রের কূলে বসে সমুদ্রকে দেখে এক মহান ভাবে আপ্লুত হই, কিন্তু দিনের পর দিন যখন দশদিকের নয়দিকে কেবল সমুদ্রই দেখি আর দশম দিকে দেখি সমুদ্র-দিগ্বলয়িত আকাশ তখন ভয়ে প্রাণ উড়ে যায়। তবু সঙ্গে লোকজন থাকে বলে ভরসা থাকে। বাইরে যত বড়ো বিপদ হাঁ করে থাকুক না কেনভিতরে তাস খেলার বিরাম নেই, কখনো নাচ চলেছে কখনো বাজি রেখে নকল ঘোড়দৌড়। ঠিক যেন কোনো একটা হোটেলে বাস করছি, পরস্পরের অতি কাছাকাছি, অথচ কারও সঙ্গে কারও গভীর সম্বন্ধ নেই। খাচ্ছি-দাচ্ছি গল্প করছি হাসি তামাশায় যোগ দিচ্ছি চটছি ও মনখারাপ করছি—তবু জানি এ দু’দিনের খেলা। একটা কৃত্রিম অবস্থার চক্রান্ত। ভূপৃষ্ঠে কেউ সমস্তক্ষণ হোটেলেও থাকে না, একাদিক্রমে এত রকম মানুষের সংস্রবেও আসে না, এদের সঙ্গে জীবনের অভিনয়ও করে না। ভূপৃষ্ঠে যা বৃহৎ জনসমষ্টির মধ্যে অথচ অল্প সংখ্যক প্রকৃত বন্ধু বা সহকর্মীর সঙ্গে সত্য, জাহাজে তা সত্যের নকল। তাই জাহাজী সামাজিকতার কথা মনে পড়লে হাসি পায়, ও সম্বন্ধে অত সিরিয়াস না হলেই ঠিক হত।
ইউরোপের অধিকার যখন ভূমধ্যসাগরের সঙ্গে শেষ হল তখন ক্রমাগত মনে উঠতে লাগল ভারতবর্ষের কথা। ভারতবর্ষের স্মৃতি সযত্নে ভুলেছিলুম, পাছে পুরাতনের মায়ায় নূতনকে অবহেলা করি, অতীতের রোমন্থন করতে বর্তমানের স্বাদ না নিই। এখন তো ইউরোপ হল অতীতের এবং বর্তমানের জাহাজী জীবন বিস্বাদ লাগছে—এখন ভারতবর্ষ আমার সোনার ভবিষ্যৎ, আমি তারই ধ্যান করব।
ভারতবর্ষের এমন একটি মূর্তি দেখতে পেলুম যা একমাত্র আমার মতো মানুষই দেখতে পায়—আমার মতো যে মানুষ ভারতবর্ষকে জন্মসূত্রে ও ইউরোপকে প্রেমসূত্রে চিনেছে, যে মানুষের মন উভয়ের সাক্ষাৎ পরিচয় পেয়ে উভয়ের যথার্থ পরিমাণ জেনেছে। সকল কলহ কোলাহলের ঊর্ধ্বে ভারতবর্ষ তাঁর যোগাসনে বসে আছেন, তাঁর নিমীল নেত্রে হাসির দ্যুতি, প্রাপ্তির আনন্দ তাঁর পার্থিব অভাবকে তুচ্ছ করেছে। সুন্দরী ইউরোপা তার যৌবনের ঐশ্বর্য নিয়ে তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে নূপুর বাজাচ্ছে, তাঁর মন পাচ্ছে না। পাবে, যদি পার্বতীর মতো তপশ্চারিণী হয়। ইউরোপকে ভারতবর্ষের যোগ্য হতে হবে। নইলে সে কেবল ভারতবর্ষকে বাইরে থেকে বাঁধতে ও বিচার করতে থাকবে এবং সেই কল্পিত আত্মপ্রসাদে স্ফীত হতে থাকবে।
বম্বেতে যখন নামলুম তখন ভারি মিষ্টি লাগল মরাঠি কুলিদের কর্মকালীন গোলযোগ। যা-ই দেখি তা-ই মিষ্টি লাগে। গাছতলায় মানুষে-গোরুতে-ছাগলে মিলে শুয়ে আছে। হিন্দু নাপিত মাটিতে বসে মুসলমানকে ক্ষৌরি করে দিচ্ছে! কাছা-দেওয়া মরাঠি মেয়ে মাথায় বিরাট বোঝা ও বগলে শিশু নিয়ে দৃপ্ত ব্যস্ততার সঙ্গে পথ চলছে। গুজরাতি মেয়ে ব্রীড়ায় ললিতগতি। ভারতবর্ষের সব প্রদেশের পুরুষ বম্বের রাজপথে প্রতিনিধি পাঠিয়েছে। সকলে সমান গম্ভীর, শান্ত, আত্মস্থ। ভারতবর্ষ এ কী নূতন রূপে দেখা দিল!
ভারতবর্ষে ফিরলুম, কিন্তু এ কোন ভারতবর্ষ! যাকে রেখে গেছলুম সে নেই। নবীন ভারতবর্ষ আমাকে না-দেখে, না-জেনে আমার অভাব বোধ না করে কোন ফাঁকে জন্মেছে ও বেড়েছে। না সে আমাকে চেনে, না আমি তাকে চিনি। তার সঙ্গে মিতালি পাতাতে হবে, সতর্ক থাকতে হবে, পাছে তার আত্মাভিমানে ঘা দিয়ে ফেলি। তার কঠিন কথা শুনে মর্মাহত হলে চলবে না। ঘরে তোলার আগে আমাকে পরখ করার অধিকার তার আছে। আমি আগন্তুক। সে গৃহস্বামী।
পুরাতন বন্ধুরা বলে, ‘কই, কিছুমাত্র পরিবর্তন দেখছি না তো! যেমনটি ছিলে তেমনিটি আছ।’ যেন মস্ত একটা পরিবর্তন ওরা আমার আকৃতিতে ও আচরণে প্রত্যাশা করছিল; নিরাশ হল। আমি বলি, ‘তা হলে তো আমাকে গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে সহজ। আমি ভেবে মরছি কী করলে তোমাদের মন পাব।’
কিন্তু সত্যিই সহজ নয়। আমি তো জানি আমি সেই আমি নই। দুটি বছরে প্রত্যেক মানুষের জীবন এক থেকে আরেক হয়ে ওঠে, প্রতিদিন দেখি বলে কোনোদিন লক্ষ করিনে। আমার সম্বন্ধে ওদের এবং ওদের সম্বন্ধে আমার ওই প্রতিদিন দেখাটুকু ঘটেনি বলে অন্তরে অন্তরে আমরা পর হয়ে পড়েছি। দুটো মহাদেশের ব্যবধান সেই বিচ্ছেদকে ঘোরালো করেছে। দু-বছর চোখের আড়ালে বেড়েছি, এইটে প্রধান। দু-বছর বিলেতে থেকেছি, এটা অপ্রধান। কিন্তু ফট করে ওরা বলে বসে, ‘একেবারে আহেল বিলেতি হয়ে ফিরেছ! আমাদের সঙ্গে মিলবে কেন?’
বিলেত ফেরতারা যে নিজেদের মধ্যে একটা সমাজ কিংবা সম্প্রদায় কিংবা আড্ডা রচনা করে সেটা এই দুঃখে। এরাও ভুলতে পারে না ওরাও ভুলতে পারে না—কয়েক বছর ও কয়েক হাজার মাইলের ব্যবধান। তার উপর বিলেত ফেরতারা সাধারণত ধনী কিংবা উচ্চপদস্থ হয়ে থাকে, অবস্থার ব্যবধান মানুষ চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে ভালোবাসে। বিলেতের সমাজেও ভারত ফেরতাদের এককালে ‘নবাব’ বলা হত। ইদানীং তাদের অবস্থার বিপর্যয় হয়েছে বলে তাদের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বলে পরিহাস করা হয়। ক্রমশ ইঙ্গবঙ্গদের কপালেও পরিহাস জুটছে।
কোথায় ভারতবর্ষ, কোথায় ইউরোপ। মাঝখানে আরব, তুর্কি, পারস্য, আফগানিস্তান ইত্যাদি কত দেশ পড়ে রইল। বিধাতা কার সঙ্গে কাকে বেঁধে দিলেন। পরিহাসই করো আর নেতৃত্বই দাও—আমাদের সংখ্যা ও প্রভাব বাড়তেই থাকবে। ভাবী ভারত ইউরোপে আমেরিকায় লক্ষ লক্ষ যুবক পাঠাবে ও তারা ফিরলে তাদেরকে ঘরে তুলবে। আমরাই ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের পূর্বপুরুষ। সেইজন্যে আমাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে আমরা সচেতন থাকব। শুধু দু-তিন বছর ইউরোপে গিয়ে ফুর্তি করে ফেরা নয়। আমাদের কাজ ইউরোপে ভারতবর্ষকে ও ভারতবর্ষে ইউরোপকে প্রকৃত ও প্রকৃষ্টরূপে পরিচিত করা। আমরা দুই মহাদেশের নুন খেয়েছি। দুই মহাদেশের কত লোক আমাদের প্রাণরক্ষা করেছে, আমাদের সেবা করে মূল্য গ্রহণ করেনি, আমাদের পরমাত্মীয় হয়ে দান-প্রতিদানের ঊর্ধ্বে উঠে গেছে। আমরাও যেন নিন্দা-বিদ্বেষ ঘৃণা-অবজ্ঞার ঊর্ধ্বে উঠে উভয় মহাদেশকে নিকট থেকে নিকটতর করে বিধাতার অভিপ্রায়কে সফল করে তুলি।
যেদিন আমি বিদেশযাত্রা করেছিলুম সেদিন শুধু দেশ দেখতে যাইনি। গেছলুম মানুষকেও দেখতে, মানুষের সঙ্গে মিশতে, মানুষের সঙ্গে নানা সম্বন্ধ পাতাতে। দেশের প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট সৌন্দর্যের চেয়ে দেশের মানুষ সুন্দর। মানুষের অন্তর সুন্দর, বাহির সুন্দর, ভাষা সুন্দর, ভূষা সুন্দর। দেশ দেখতে ভালো লাগে না যদি দেশের মানুষকে ভালো না লাগে। কে যেন বলেছেন, ‘এদেশের সব সুন্দর, কেবল মানুষ কুৎসিত।’ তিনি দূর থেকে মানুষকে দেখে ও-কথা বলেছেন, কাছে গিয়ে দেখেননি। যে-দেশে যাও সেদেশে দেখবে মানুষের চেয়ে সুন্দর কিছু নেই, মানুষের সৌন্দর্যের ছোঁয়া লেগে বুঝি বাকি সব সুন্দর হয়েছে! প্রকৃতি মানুষের হাতে-গড়া প্রতিমা না হোক মানুষের প্রাণের রসে রসায়িত এবং ধ্যানের দ্বারা প্রভাবিত। প্রকৃতি তো মানুষেরই প্রতিকৃতি; বিশেষ করে ইউরোপে।
ভারতবর্ষকে রবীন্দ্রনাথ মহামানবের সাগরতীর বলেছেন। ইউরোপকে আমি বলব মহামানবের মানস সরোবর। সাগরে যেমন সকল প্রবাহিণী মিলিত হয়, মানস সরোবর থেকে তেমনি সকল প্রবাহিণী নির্গত হয়। ইউরোপের মানস থেকে যুগে যুগে কত ভাবধারা নিঃসৃত হয়ে পৃথিবীকে ভাবোর্বরা করেছে। পৃথিবী নিজেই তো পৃথিবীর প্রতি ইউরোপের দান, কারণ পৃথিবী ইউরোপের আবিষ্কার। কেই-বা জেনেছিল আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকার অস্তিত্ব? পৃথিবীর আকার, আকৃতি, গতি ও অবস্থান ইউরোপই আমাদের জানাল। আমরা পরলোকের নাড়িনক্ষত্র জানতুম কিন্তু যে-লোকে জন্মেছি তার সম্বন্ধে বড়োজোর এই জানতুম যে, সেটাকে একটা সাপ নিজের ফণার উপরে অতি যত্নে ব্যালান্স করে একটা হাতির পিঠের উপর অতি কষ্টে টাল সামলাচ্ছে।
সত্যের একটি বিন্দুও নষ্ট হবার নয়। ইউরোপের সত্য ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতেই হবে, ভারতবর্ষের সত্য ইউরোপকে। দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে মহামিলনের লগ্ন আসবেই। কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ। আজ যা আসেনি কোনো একদিন তা আসবে বলেই আজ আসেনি। কিন্তু সে আমাদের সকলের ভাবনা, সকলের স্বপ্ন; আমার একার নয়। আমি ভাবি আবার কবে ইউরোপের সঙ্গে মিলিত হব, কথা রাখব!
দিনের পর দিন যায়। ইউরোপের স্মৃতি অস্পষ্ট হতে থাকে। সত্যি কি কোনোকালে ইউরোপে ছিলুম!
***
* ফ্রান্সের গভর্নমেন্টে একজন মিনিস্টার অব ফাইন আর্টস থাকেন, ইংল্যাণ্ডে সেরূপ নেই, ইংরেজরা সব বিষয়ের মতো এ বিষয়েও প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজের পক্ষপাতী।
* যে সমাজ দুর্ভিক্ষও চায় না যুদ্ধও চায় না সে সমাজের তৃতীয় পন্থা জন্মশাসন। গান্ধীমার্কা জন্মশাসনে দুর্ভিক্ষের ভাব আছে— অজাত প্রাণীর পক্ষে তা সম্ভাব্যতার মৃত্যু। ষ্টোপসমার্কা জন্মশাসনে যুদ্ধের ভাব আছে—অজাত প্রাণীর পক্ষে তা সম্ভাব্যতার হত্যা। কিন্তু যে সমাজ না চায় দুর্ভিক্ষ না চায় যুদ্ধ না চায় কোনো প্রকার জন্মশাসন, সে সমাজের আবদার প্রকৃতির অসহ্য।
* একটি সমিতির সেক্রেটারি লিখছেন, ‘আপনি কি জানেন যে আমাদের বনফুলগুলি একে একে লোপ পেয়ে যাচ্ছে? তাদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে এই সমিতির প্রয়াস ও উপায় উদ্ভাবনে আপনি যোগ দেবেন?’
* H টি হচ্ছে আর্থার খুড়োর এক ছেলে। খুড়োর আরেক ছেলে আরেক জায়গায় জিতেছেন। খুড়োর নাম তো জানে বিশ্বের সব জনে, আমাদের সেই তাহার নামটি বলব না।
* কেউ তার শ্যালিকাকে বিবাহ করতে পারবে কি না, শ্যালিকাকন্যাকে বিবাহ করতে পারবে কি না পার্লামেন্ট এ সম্বন্ধে বিধান দেয়। আগে ছিল চার্চের এলাকা, এখন চার্চের অধীনে আদালত নেই।
* এ ছাড়া আধা উপরে আধা নীচের রেলস্টেশন উনচল্লিশটা।
* তাঁর অসংখ্য সুপাত্রীর কারুকে বিবাহ না করে অ্যারিস্টোক্র্যাট তিনি বিবাহ করলেন কিনা এক চাষানিকে, তাও বহুকাল একসঙ্গে বাস করবার পরে। এর অর্থ কি এই নয় যে তিনি চীনেমাটির পুতুলের কাছে যা পেতেন তার বেশি পেয়েছিলেন মাটির মেয়ের কাছে? প্রকৃতির হাতে-গড়া প্রাণময়ী নারীর কাছেই মনোময় পুরুষের পরিপূরকতা।