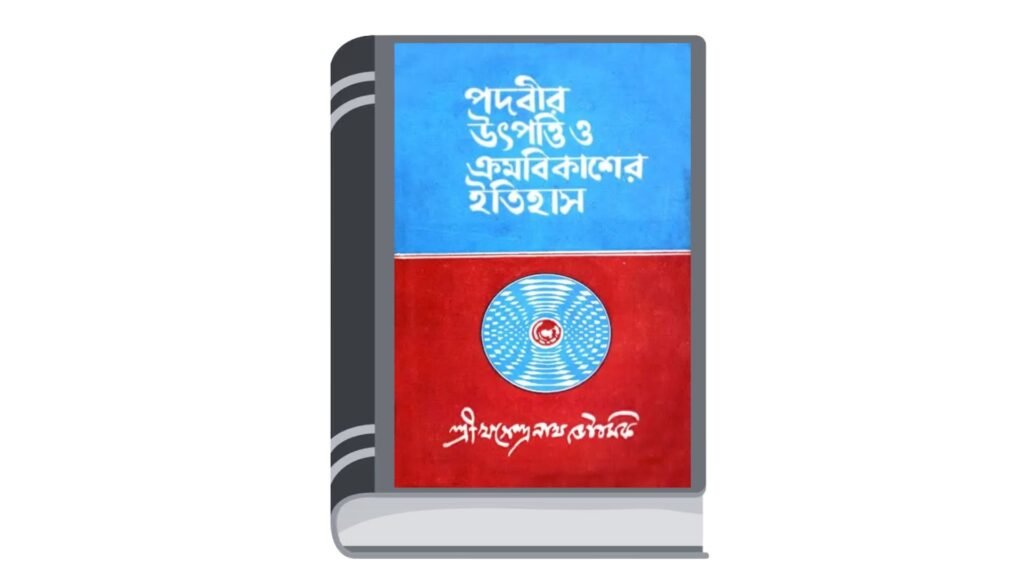সমাজ-বিবৰ্তন
প্রাক্-বর্ণবিভাগ যুগে এক আর্য পিতার বিভিন্ন সন্তান বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাদের বৃত্তিবাচক কোন পরিচয় বা ভাগ ছিল না। পরে বিভিন্ন বৃত্তিকে জ্ঞান, শৌর্য, অর্থ ও সেবা এই চারটি ভাগে ভাগ করে এই সব বৃত্তি গ্রহণকারীদের বৃত্তি বা কর্মভিত্তিক ভাগে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নামে চতুর্বর্ণে ভাগ করা হয়। (বর্ণের এক অর্থ গুণ; গুণানুসারে প্রত্যেককে উক্ত বৃত্তি বা কর্মের জন্য বরণ করা হল)। গুণের দ্বারা কর্ম প্রাপ্তি সাধারণ অর্থে কর্মে দক্ষতা বা কর্মপটুতা বুঝায়। কিন্তু গুণের অপর অর্থ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন প্রাকৃতিক গুণ। প্রত্যেক ব্যক্তিরই প্রাকৃতিক তিনগুণের একটি না একটির প্রাধান্য থাকে এবং সেই গুণাশ্রয়ী কর্মে ব্যক্তির কর্মদক্ষতা দিন দিন বৃদ্ধি পায়। জ্ঞান, শৌর্য, অর্থ ও সেবা কর্ম গুলিতে উক্ত প্রাকৃতিক গুণের প্রভাবে কর্মদক্ষতা বা পটুতাই বর্ণ সৃষ্টির সূত্ররূপে গৃহীত হয়ে থাকে। সত্ত্বগুণ সম্পন্ন সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক যাঁরা, তাঁরা মুক্তসংগ, অহংবাদশূন্য, ধৃতিমান, উৎসাহী ও সিদ্ধাসিদ্ধ বিষয়ে নির্বিকার ত্যাগী পুরুষ। যাঁরা রজোগুণ সম্পন্ন রাজসিক প্রকৃতির লোক তাঁরা প্রভুত্ব, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, সম্মুখসম্পদের অভিলাষী। তমোগুণ সম্পন্ন তামসিক প্রকৃতির মানষ অত্যধিক নিদ্রা, আলস্য, ভয় ও মূঢ়তায় আচ্ছন্ন। প্রকৃতির এই তিন গুণভেদ অনুযায়ী মানুষের কর্মক্ষেত্রও মূলত তিন প্রকার। আর ঐ গুণগত কর্মভেদ অনুযায়ী হিন্দু ধর্মে বর্ণের সৃষ্টি হয়েছে। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যথাশাস্ত্র ধর্মানুশীলন, যাগযজ্ঞ সমাপন ও ‘সর্বজনহিতায়’ কর্মে পৌরোহিত্য করণ সত্ত্বগুণে সম্পন্ন ব্রাহ্মণের কর্ম। রজোগুণজাত প্রভুত্ব, ক্ষমতালোভ, সুখসম্পদ ভোগ, দেশরক্ষা, দেশের শান্তিরক্ষা ও প্রয়োজনবোধে যুদ্ধবিগ্রহ করা ক্ষত্রিয়ের কর্ম’। আর, রজোগণের আধিক্য ও তমোগণের অল্পতায় কৃষি ও বাণিজ্য দ্বারা দেশের ধনবৃদ্ধি বৈশ্যের কর্ম। কায়িক শ্রমের দ্বারা অন্য তিন বর্ণকে তাদের নিজ নিজ কর্মে সাহায্য করাই তমোগুণ সম্পন্ন শূদ্রের কর্ম। উক্ত প্রাকৃতিক গুণত্রয়ের প্রত্যেকটি গুণই অভ্যাস ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে বর্ধিত বা হ্রাসপ্রাপ্ত হতে দেখা যায়।
উল্লেখিত গুণগত কর্মভেদের চারটি ভাগের অন্যতম জ্ঞানবলের প্রতীক ব্রাহ্মণ তাঁদের জ্ঞান, বৃদ্ধি, অহংভাবশূন্যতা প্রভৃতি সত্ত্বগুণের বলে সমাজকে পরিচালিত করতেন। সমাজের সবাই তাঁদের মুখের কথায় চলত বলে তাঁরা সমাজরূপী বিরাটের মুখস্বরূপ। শৌর্য বা বাহুবলের প্রতীক ক্ষত্রিয়—তাঁরা মূলত রজোগুণের অধিকারী বলে তাঁদের বাহুবল দ্বারা সমাজের রক্ষণাবেক্ষণ বা শান্তিরক্ষা করতেন। সমাজেকে রক্ষা করতেন বলেই তাঁরা সমাজরূপী বিরাটের বাহুস্বরূপ। ধনবলের প্রতীক বৈশ্য প্রধানত রজোগুণান্বিত–তাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা ধনের সংস্থানে লিপ্ত থাকতেন। উরু যুগল যেমন উদরকে ধারণ করে সেইরূপ সমাজের উদর পোষণে লিপ্ত থাকতেন বলেই তাঁরা সমাজরূপী বিরাটের উরুস্বরূপ। আর শ্রমবলের প্রতীক শূদ্র তমোগুণাগত; তাঁরা কায়িক শ্রমের দ্বারা অন্য তিন বর্ণের কর্মের সহায়তা করতেন। পদযুগলকে নির্ভর করে উরু, উদর ও মস্তিষ্ক দণ্ডায়মান বলেই তাঁরা সমাজরূপী বিরাটের পদযুগল স্বরূপ। এখানে সমাজকে বিরাটত্বে স্থান দিয়ে তার সেবায় চারটি কর্মের দ্বারাই চতুর্বর্ণের উৎপত্তি প্রতিপন্ন। কিন্তু ব্রহ্মার মুখ হতে ব্রাহ্মণের, বাহু হতে ক্ষত্রিয়ের, উরু হতে বৈশ্যের ও পদ হতে শূদ্রের উৎপত্তি, এই মতের যৌক্তিকতা গ্রহণযোগ্য কিনা তা ভাববার বিষয়। কারণ, চতুর্বেদের মধ্যে ঋগ্বেদ আর্য তথা হিন্দুদের প্রাচীনতম গ্রন্থ, এবং তাতে গুণভিত্তিক চতুর্বর্ণ সৃষ্টির কথা উল্লেখ আছে; আর, বৈদিক যুগের অনেক পরে ঋগ্বেদ সংহিতায় “ব্রহ্মার মুখ হতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি” ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা গুণগত কর্মভেদের স্থলে জন্মগত অধিকারের কথা পরিলক্ষিত হয়। এবংবিধ বিভিন্ন মতগুলি গবেষকদের গবেষণার বিষয়।
কর্মের দ্বারা চারটি বর্ণের সৃষ্টি হলেও তখন উহা জন্মগত ছিল না—গুণকর্মভিত্তিক ছিল। বর্ণে বর্ণে গুণকর্মভিত্তিক বর্ণে বর্ণে যে কোন বিভেদ ছিল না তা নিম্নোক্ত আলোচনাদিতে প্রতীয়মান—প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণপুত্র গুণভ্রষ্টতায় এবং কর্ম বা বৃত্তিতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রেরূপে খ্যাত হয়েছেন এবং শূদ্রতনয়ও গুণগত উৎকর্ষের জন্য ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছেন। দাসীপুত্র কবষও একজন বৈদিক ঋষি হয়েছিলেন এবং “ভর্তৃহীনা জবালার” পুত্র সত্যকামও “দ্বিজোত্তম” ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ আরও বলা যায়, বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় কুলে জন্মগ্রহণ করেও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন। আবার, পরশুরাম ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করলেও কর্মে’র জন্য ক্ষত্রিয় বলে পরিগণিত হন।
ব্রাহ্মণ গুণগত বৈশিষ্ট্যে বর্ণের শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য হলেও তার ক্ষত্রিয়াদি ত্রিবর্ণের অন্ন গ্রহণের কোন নিষেধবিধি যে ছিল না তার প্রমাণ বহু পুরাণ ও সংহিতায় দেখতে পাওয়া যায়। যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, বিষ্ণু, ও যম প্রভৃতি সংহিতায় এবং অগ্নি, আদিত্য ও কূর্ম প্রভৃতি পুরাণে এইরূপ বিধানের উল্লেখ আছে। বাস্তবক্ষেত্রেও অনুরূপ সামাজিক ব্যবহার ছিল। বর্ণগুলির পরস্পরের মধ্যে বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল,—ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা; ক্ষত্রিয়েরা বৈশ্যা, শূদ্রা; বৈশ্যেরা শূদ্রা পত্নী গ্রহণ করলে তা অনুলোম; আর, ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণী; বৈশ্যেরা ক্ষত্রিয়া বা ব্রাহ্মণী; শূদ্ররা বৈশ্যা, ক্ষত্রিয়া বা ব্রাহ্মণী পত্নী গ্রহণ করলে তাকে প্রতিলোম বিবাহ বলা হত। শাস্ত্র পুরাণে অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহের দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বর্ণগুলির মধ্যে স্পর্শদোষ ছিল না। শাস্ত্রবিধি অনুসারে শূদ্র পাচকের রান্না-করা অন্নাদি অন্য বর্ণের হিন্দুরা ভক্ষণ করতেন। মনু-সংহিতায় আছে, দাস্যকর্ম দ্বারা জীবিকা অর্জনে অক্ষম হলে শূদ্র পাচকের বৃত্তি গ্রহণ করে তার পরিবার প্রতিপালন করবে।
আর্যগণের গুণভিত্তিক বর্ণবিভাগ কালক্রমে বর্ণকেন্দ্রিক ও বংশভিত্তিক হয়ে দাঁড়ানোর মূলে রয়েছে ঐ চতুর্বর্ণের প্রত্যেক পরিবারের সন্তানদের প্রতি পিতৃপুরুষের অপত্যস্নেহ এবং সন্তানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অভিভাবনা। ফলে ব্রাহ্মণ তাঁর সন্তানদের বেদ অধ্যয়ন করাতেন এবং নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত করে তুলতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু যে-সন্তান ব্রাহ্মণের গুণের অধিকারী হতে পারতেন না কালক্রমে তিনিও ব্রাহ্মণরূপে স্বীয় বর্ণের সর্বকর্মের অধিকারী হতে লাগলেন। অনুরূপভাবে, ক্ষত্রিয়গণ তাঁদের সন্তানদের যদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করে তুলতে চেষ্টা করতেন কিন্তু কোন ক্ষত্রিয়নন্দন যুদ্ধ বা শাসনকার্যে পারদর্শিতা দেখাতে না পারলেও ক্ষত্রিয়রূপে পরিচিত হতেন। একইভাবে, অনুপযুক্ত হয়েও বৈশ্যের ছেলে বৈশ্য ও শূদ্রের ছেলে শূদ্র বলেই পরিচিত হতেন। এইরূপে প্রত্যেক বর্ণই নিজ নিজ কর্মগত স্বার্থ রক্ষায় সতত তৎপর থাকতেন। ফলত গুণভিত্তিক বর্ণ বিভাগের অবকাশ রইল না। তবে তখনকার সমাজব্যবস্থায় বর্ণভিত্তিক কর্মবিভাগ থাকার ফলে বংশগত কর্মে— নৈপুণ্য অর্জনের সংযোগ স্বভাবতই প্রত্যেক বর্ণের সন্তানেরা পেত। কিন্তু পরবর্তীকালে নূতন ও পরিবর্ধিত সমাজব্যবস্থায় পূর্বের সুফলদায়ক গুণগত বর্ণবিভাগের স্থলে দেখা দিল জন্মের অধিকারে বর্ণের অধিকার এবং বর্ণের অধিকারে কর্মের অধিকার। সমাজস্বার্থের উপরে স্থান পেল সংকীর্ণ পারিবারিক স্বার্থ বা ব্যক্তিস্বার্থ। এবং ফলত বর্ণে বর্ণে গড়ে উঠল বিরাট ব্যবধান ও বিভেদের প্রাচীর। স্বার্থান্ধ মানুষের দ্বারা জ্ঞান, শৌর্য, অর্থ ও সেবা, কর্মের এই চারটি মূলভাব চতুর্বর্ণের গণ্ডিতে আবদ্ধ হওয়াতে বর্ণে বর্ণে বিভেদ সৃষ্টি হয়েই শেষ হল না; অতঃপর ঐ কর্মগুলির স্তর, শাখাস্তর ও বিভিন্ন উপস্তরে কর্মরত মানুষগুলিকে চিহ্নিত করা হল এক একটি পৃথক জাতের মানুষরূপে। এইরূপে বিভিন্ন কর্ম বা বৃত্তি অবলম্বনকারীরা তাদের বংশানুক্রমিক প্রথার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন জাতে পরিণত হল। ক্রমে জাতিগত কর্মগুলির বিভিন্ন স্তরে মানানুযায়ী উচ্চ-নীচ নির্দিষ্ট হতে লাগল। আর, এর ব্যাপক প্রসারের ফলে দেখা দিল জাতপাতের ভেদ-বিচার। এবং জন্মসূত্রে বর্ণ ও শ্রেণী নির্ধারণের সরল ব্যবস্থার ফলে মানুষের সহজাত বৃত্তি এবং স্বাভাবিক গুণ বিকাশের আর কোন সুযোগ রইল না।
আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকের শেষ অবধি বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য ছিল। এই বৌদ্ধ ধর্ম জাতিভেদ এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে বিশেষ আঘাত হেনেছিল; ফলে জাতিভেদের কঠোরতা অনেকটা শিথিল হয়ে এসেছিল। দীর্ঘদিন ধরে বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য এবং বিশেষত বৌদ্ধ শাসনের ফলে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য বা জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা না থাকায় উচ্চ-নীচ জাতপাতের ভেদাভেদ ছিল না। অসবর্ণ বিবাহের বহুল প্রচলন হয়েছিল। বৌদ্ধ রাজশাসন ও ধর্মের প্রভাবে চতুর্বর্ণের মধ্যে পংক্তিভোজন ইত্যাদি প্রথা প্রবর্তিত হয়েছিল।
খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকেই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থান সুরু। আর, তখন থেকেই বঙ্গদেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব স্তিমিত হতে থাকে। অবশ্য পাল রাজাদের আমল অবধি বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল। কারণ, পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ। সেন রাজাদের শাসনকালে আবার হিন্দু সমাজের পুনর্গঠন আরম্ভ হয়। এই পুনর্গঠনের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন রাজা বল্লালসেন। তাঁর রাজসভায় নানা শাস্ত্রে বিশারদ বড় বড় পণ্ডিতের সমাবেশ হয়েছিল। তাঁদের সাহায্যে হিন্দু সমাজে পুনরায় জাতিভেদ প্রথা প্রবর্তিত হয়। বল্লালসেন যে শুধু হিন্দু সমাজের পুনর্গঠন করলেন তা-ই নয়, কর্মভেদ অনুযায়ী এমনভাবে নূতন ৩৬টি জাত বা শ্রেণীর সৃষ্টি করেছিলেন যাতে সমাজে বিভেদের সূচনা হল। এবং শ্রেণীতে শ্রেণীতে উচ্চনিম্নবোধ তথা প্রভেদ অনেক বেড়ে গেল। এককথায়, বিষবৃক্ষের বীজ রোপিত হল।
এই বীজ থেকে অংকুরিত বিভেদের বিষবৃক্ষ মহীরুহে পরিণত হয়ে তার শাখা-প্রশাখা ছড়াল। হিন্দু সমাজে দেখা দিল শ্রেণী, গোষ্ঠী, স্পৃশ্য, অস্পৃশ্য ইত্যাদি কত কী রকমারি বিভেদ। ব্রিটিশ ভারতের প্রথম আদমশুমারীতে দেখা যায়, ভারতে প্রায় চার হাজার শ্রেণীর লোক বাস করত। হিন্দু সমাজে ছুৎমার্গ এবং পতিত ও দৃষ্ট শ্রেণী ঠিক কখন দেখা দেয় তার প্রামাণিক কাল উল্লেখ করা না-গেলেও বলা যায় যে, বঙ্গদেশে সেন রাজাদের আমল থেকেই এর ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। সেন রাজাদের সময়ে বৌদ্ধধর্মে যখন ভাঁটার টান এবং হিন্দু ধর্মে এসেছে জোয়ারের স্রোত তখন থেকে বৌদ্ধরা দলে দলে হিন্দু সমাজে ফিরে আসতে লাগল।
যারা প্রথমেই এল তাদের সমাদরেই গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু যারা এল না অথবা দুই-এক পুরুষে পরে কিংবা আরও বেশি বিলম্বে হিন্দু সমাজে প্রত্যাবর্তন করল তাদের পর্যায়ক্রমে বিচার করে অনাচরণীয়, ভ্রষ্ট, পতিত, অস্পৃশ্য ইত্যাদি শ্রেণীর লোক বলে গণ্য করা হল। এবং সমাজে এরা পতিত বলেই থেকে গেল। রাজবংশের উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু সমাজের পুনরায় উত্থান ও পুনর্গঠন হল এবং কেবলমাত্র জন্মাধিকারে ব্রাহ্মণগণ শ্রেষ্ঠ বর্ণরূপে শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকাণ্ডের অদ্বিতীয় বিধায়ক, হোতা, ধারক ও বাহকরূপে নির্দিষ্ট হলেন। গুণাশ্রয়ী কর্মভিত্তিক বর্ণ বিভাগের সহযোগ সমাজে না-থাকায় উল্লেখিত অনাচরণীয়, ভ্রষ্ট, পতিত ও অস্পৃশ্যরূপে চিহ্নিত মানুষগুলির যাঁরা নিজ গুণ ও সাধনায় ব্রাহ্মণ ও উন্নত পর্যায়ের জাতিগগুলির সমকক্ষ তারাও অবহেলিত এমনকি ঘৃর্ণিত থেকে গেলেন। হিন্দু শাস্ত্রকারদের নানা প্রকার কঠোর বিধানে এবং সেন রাজাদের সময় থেকে হিন্দু সমাজে সেই সব অননুশাসনগুলি কঠোরতর ভাবে প্রয়োগের ফলে ব্রাহ্মণবর্ণসহ সকল উন্নত পর্যায়ের জাতগুলির শ্রেণীস্বার্থ ও বিশেষভাবে ব্রাহ্মণদের প্রভুত্ব বজায় থাকল বটে কিন্তু সমাজে বিভেদ শতগুণে বর্ধিত হল। এইভাবে দীর্ঘদিন চলার পর ব্রিটিশ শাসনে দেশে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রবর্তন ও তার প্রভাব হিন্দু সমাজে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দেয়। বঙ্গদেশে তথা ভারতের অন্যান্য প্রদেশে স্কুল-কলেজগুলিতে সমাজের সর্বশ্রেণীর জনগণই শিক্ষার স্বাধীনতা ও সংযোগ লাভ করায় তথাকথিত অনাচরণীয়, ভ্রষ্ট, পতিত ও অস্পৃশ্যরূপে চিহ্নিত জাতের মানষগুলিও নিজেদের শিক্ষিত ও নানাভাবে যোগ্য করে তোলার সুযোগ লাভ করেন। এবং ক্রমে তাঁদের পূর্বের শ্রেণীগত নির্দিষ্ট কর্মের গন্ডি ছাড়িয়ে যোগ্যতা অনুসারে বিভিন্ন সম্মানজনক কর্মে নিয়োজিত হতে থাকেন। পক্ষান্তরে, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উন্নত শ্রেণীগুলির অশিক্ষিত ও অযোগ্য লোকদেরও সাধারণ কর্ম গ্রহণ করতে হয়। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে গুণ বা যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় কর্মের দ্বারা সমাজের তথাকথিত উন্নত ও অনুন্নত লোককে চিহ্নিত করার সুযোগ আজ অবলুপ্তির পথে। তবে একদা যে কর্মদক্ষতা বা যোগ্যতা কর্মভিত্তিক চতুর্বর্ণ বিভাগের সূত্ররূপে গৃহীত হয়েছিল সেই কর্মদক্ষতা বা যোগ্যতার মাপকাঠিতে বিভিন্ন স্তরে কর্মে নিযুক্ত লোকদের জন্য নূতন করে সমাজ গঠন হচ্ছে বা হবে কিনা তা সমাজবিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয়।