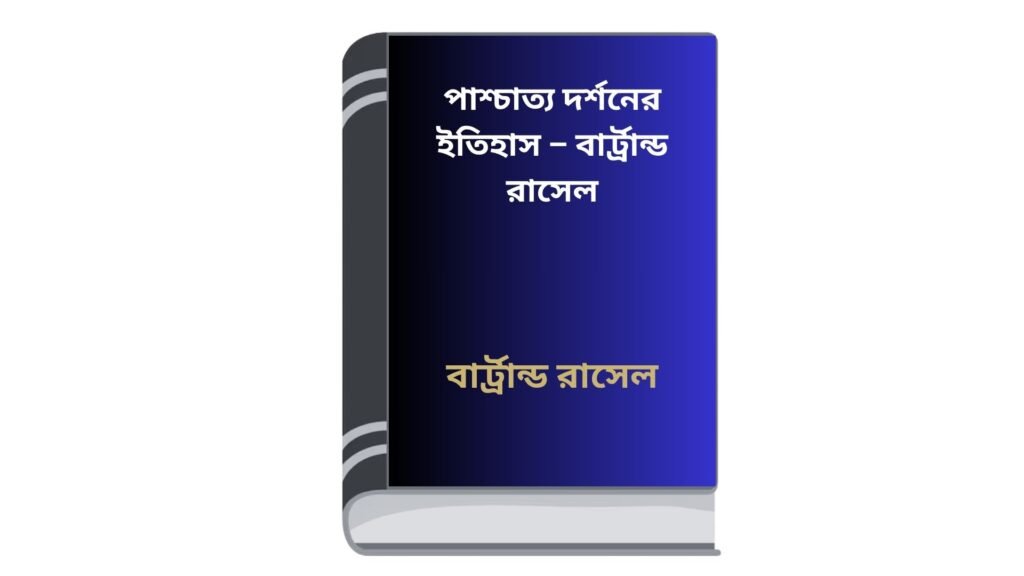২৫. হেলেনায়িত যুগ
তৃতীয় খণ্ড — আরিস্ততেলেস পরবর্তী প্রাচীন দর্শন
২৫. হেলেনায়িত যুগ
আদি কালের গ্রিক-ভাষী জগতের ইতিহাসকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে- স্বাধীন নগররাষ্ট্রের যুগ, এই যুগের অবসান ঘটান ফিলিপ এবং আলেকজান্দ্রস; মাকেদনীয় প্রভুত্বের যুগ, এর শেষ চিহ্ন নির্বাপিত হয় ক্লিওপেট্রার মৃত্যুর পর মিশর রোমক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে এবং অন্তিমে রোমক সাম্রাজ্যের যুগ। এই তিনটি যুগের মধ্যে প্রথমটির বৈশিষ্ট্য ছিল স্বাধীনতা এবং বিশৃঙ্খলা আর দ্বিতীয়টির বৈশিষ্ট্য ছিল পরাধীনতা এবং বিশৃঙ্খলা, তৃতীয়টির বৈশিষ্ট্য ছিল পরাধীনতা এবং শৃঙ্খলা।
এই যুগগুলোর দ্বিতীয়টিই হলো হেলেনায়িত যুগ। বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রে এই যুগে যে কাজ হয়েছে তা সর্বযুগের গ্রিক কৃতিত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। দর্শনশাস্ত্রের এপিকুরীয় ও স্টোইক সম্প্রদায়ের ভিত্তিস্থাপন এর অন্তর্ভুক্ত এবং রয়েছে নির্দিষ্ট নিশ্চিত মতবাদরূপে গঠিত সন্দেহবাদ (scepticism)। সুতরাং এই যুগ দর্শনের ক্ষেত্রে এখনও গুরুত্বপূর্ণ, প্লাতন এবং আরিস্ততলেসের যুগের মতো না হলেও। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে গ্রিক দর্শনে সত্যিকারের নতুন কিছু হয়নি খ্রিষ্টিয় তৃতীয় শতাব্দীতে নব প্লাতনীয়দের (Neoplatonists) আবির্ভাব ছাড়া। কিন্তু এরই মধ্যে রোমক জগৎ খ্রিষ্টধর্মের বিজয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।
আলেকজান্দ্রসের সংক্ষিপ্ত কর্মজীবন হঠাই গ্রিক জগতে রূপান্তর নিয়ে এল। খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩৪-৩২৪, এই দশ বছরে তিনি এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, মিশর, ব্যাবিলনিয়া, পারস্য, সমরখন্দ, ব্যাকট্রিয়া ও পাঞ্জাব জয় করেন। পারসিক সাম্রাজ্য তদানীন্তন বিশ্বের জানিত বৃহত্তম সাম্রাজ্য ছিল, তিনটি যুদ্ধে সেই সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়। ব্যাবিলনিয়ার প্রাচীন জ্ঞান ও তাঁদের প্রাচীন কুসংস্কার কৌতূহলী গ্রিক মানসে পরিচিত হল, পরিচয় হলো জরাথুস্টবাদীদের দ্বৈতবাদের সঙ্গে এবং (স্বল্পতর পরিমাণে) ভারতীয় ধর্মগুলোর সঙ্গে, ভারতে তখন বৌদ্ধধর্ম প্রাধান্যলাভ করার মুখে। আফগানিস্তানের পর্বতেই হোক কিংবা ইয়াক্সার্তেস (Jaxartes) নদীর তীরে হোক কি সিন্ধুনদের উপনদীর পারেই হোক- আলেকজান্দ্রস যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই গ্রিক নগর প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেখানেই তিনি খানিকটা স্বায়ত্তশাসনসমেত গ্রিক প্রতিষ্ঠানের মতো প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। যদিও তার সৈন্যবাহিনীতে প্রধানত মাকেদনীয়রা ছিলেন এবং যদিও ইয়োরোপীয় গ্রিকরা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন অনিচ্ছাসত্ত্বে, তবুও তিনি প্রথম নিজেকে ভাবতেন হেলেনবাদের প্রচারক। যাই হোক, বিজিত অঞ্চলের আয়তনের ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি গ্রিক এবং বর্বরদের বন্ধুত্বপূর্ণ মিলনের নীতি গ্রহণ করলেন।
এ ব্যাপারে তাঁর নানা উদ্দেশ্য ছিল। একদিকে স্পষ্টতই তাঁর সৈন্যবাহিনী অতি বিশাল না হওয়ায় এত বিশাল সাম্রাজ্য গায়ের জোরে চিরকাল দখলে রাখতে পারবেন না এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে অবশ্যই নির্ভর করতে হবে বিজিত জনসাধারণের শুভেচ্ছার উপর। অন্যদিকে, পূর্বদেশের লোকেরা একমাত্র ঐশ্বরিক রাজা ছাড়া অন্য কোনো শাসনব্যবস্থায় অভ্যস্ত ছিলেন না, আলেকজান্দ্রস এই ভূমিকা পালনে নিজেকে দক্ষ মনে করেছিলেন। তিনি নিজেকে দেবতা বলে বিশ্বাস করতেন, না শুধু কৌশল হিসেবে ঐশ্বরিক উপাধি গ্রহণ করেছিলেন- এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে শুধুমাত্র মনস্তত্ত্ববিদ, কারণ, ইতিহাসের সাক্ষ্য এক্ষেত্রে সিদ্ধান্তমূলক নয়। সে যাই হোক, মিশরের ফারাওদের উত্তরাধিকারী হিসেবে ও পারস্যে মহান সম্রাট হিসেবে প্রাপ্ত খোসামোদ স্পষ্টতই আলেকজান্দ্রস উপভোগ করতেন। তাঁর মাকেদনীয় ক্যাপ্টেনরা- যাঁরা সাথী (companions-কম্প্যানিয়ন) নামে অভিহিত ছিলেন, আলেকজান্দ্রসের প্রতি তাঁদের আচরণ ছিল পাশ্চাত্য দেশের অভিজাতদের নিজেদের শাসনতন্ত্রসম্মত রাজার সঙ্গে আচরণের সমতুলঃ তারা ভূমিতে উপুড় হয়ে শুয়ে আলেকজান্দ্রসকে প্রণাম করতে অস্বীকার করতেন, তাঁরা জীবন বিপন্ন করেও পরামর্শ দিতেন ও সমালোচনা করতেন এবং সঙ্কটমুহূর্তে রাজার ক্রিয়াকর্ম নিয়ন্ত্রণ করতেন। গঙ্গাজয়ের অভিযানে না গিয়ে সিন্ধু থেকেই দেশে ফিরতে তাঁরা তাঁকে বাধ্য করেছিলেন। প্রাচ্যদেশীয়রা ছিলেন অনেক বেশি সহনশীল অবশ্য যদি তাদের ধর্মীয় সংস্কার মেনে চলা হতো। এর ফলে আলেকজান্দ্রসের কোনো অসুবিধা হতো না, শুধু প্রয়োজন ছিল অ্যামন (Ammon) কিংবা বেল (Bel)-কে জিউসের সঙ্গে অভিন্ন বলে মেনে নেওয়া এবং নিজেকে দেবতার পুত্র বলে ঘোষণা করা। মনস্তত্ত্ববিদদের পর্যবেক্ষণে আলেকজান্দ্রস ফিলিপকে ঘৃণা করতেন এবং হয়তো তিনি ফিলিপকে হত্যার গোপন ষড়যন্ত্রের অংশ ছিলেন। গ্রিক পুরাণের কিছু মহিলার মতো তাঁর মা অলিম্পিয়াস (Olympias) একজন দেবতার প্রেমাস্পদ ছিলেন- এরকম বিশ্বাস করতে তিনি হয়তো ভালোবাসতেন। আলেকজান্দ্রসের কর্মজীবন এমনই অলৌকিক ছিল না, তিনি ভাবতেই পারতেন তাঁর অসাধারণ সাফল্যের কারণ অলৌকিক জন্ম।
বর্বর জাতিদের তুলনায় নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ধারণা গ্রিকদের ভিতর খুবই প্রবল ছিল, আরিস্ততেলেস যখন বলছেন উত্তরের জাতিরা তেজস্বী, দক্ষিণের জাতিরা সুসভ্য এবং শুধুমাত্র গ্রিকরাই সুসভ্য ও তেজস্বী তখন তিনি নিঃসন্দেহে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশ করছেন। প্রাতন এবং আরিস্ততেলেস দুজনেই ভেবেছন গ্রিকদের ক্রীতদাস করা অন্যায় কিন্তু বর্বরদের নয়। আলেকজান্দ্রস ঠিক গ্রিক ছিলেন না, তিনি চেষ্টা করেছিলেন এই শ্রেষ্ঠত্বের দৃষ্টিভঙ্গি ভাঙতে। তিনি নিজে দুজন বর্বর রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন এবং তার অধীনস্থ নেতৃস্থানীয় মাকেদনীয়দের অভিজাত পারসিক। রমণী বিয়ে করতে বাধ্য করেছিলেন। অনুমান করা যায় তাঁর অসংখ্য গ্রিক নগরীতে স্ত্রী অভিবাসীদের তুলনায় পুরুষ অভিবাসীর সংখ্যাধিক্য ছিল, সুতরাং এই পুরুষরা নিশ্চয়ই স্থানীয় রমণীদের বিয়ে করার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছিলেন। এই নীতির ফল ছিল চিন্তাশীল মানুষের মনে মনুষ্যজাতির সার্বিক একত্বের কল্পন নিয়ে আসা। নগর রাষ্ট্রের প্রতি প্রাচীন আনুগত্য এবং (স্বল্পতর পরিমাণে) গ্রিক জাতির প্রতি আনুগত্য আর যথেষ্ট মনে হয়নি। দর্শনশাস্ত্রে এই বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি শুরু করেছিলেন স্টোইকরা কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এর শুরু আলেকজান্দ্রসের সঙ্গে। এর ফল-গ্রিক এবং বর্বরদের মেলামেশা হয়েছিল পারস্পরিক : বর্বররা শিখেছিল গ্রিক বিজ্ঞানের কিছু কিছু আর গ্রিকরা শিখেছিলেন বর্বরদের কুসংস্কারের অনেকটা। গ্রিক সভ্যতা বিস্তৃততর অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়াতে এর বিশুদ্ধতা খানিকটা হ্রাস পেয়েছিল।
গ্রিক সভ্যতা ছিল মূলত নগরকেন্দ্রিক। কৃষিকর্মে নিযুক্ত অনেক গ্রিক নিশ্চয়ই ছিলেন কিন্তু হেলেনীয় সংস্কৃতির বিশেষত্বে তাদের অবদান ছিল সামান্যই। মিলেশীয় গোষ্ঠীর সময় থেকে শুরু করে যে গ্রিকরা বিজ্ঞানে, দর্শনে ও সাহিত্যে প্রধান ছিলেন তাঁরা সংযুক্ত ছিলেন সম্পন্ন বাণিজ্যপ্রধান নগরগুলোর সঙ্গে, সেই নগরগুলো তারা সংযুক্ত ছিলেন সম্পন্ন বাণিজ্যপ্রধান নগরগুলোর সঙ্গে, সেই নগরগুলো প্রায়শ বর্ববরবেষ্টিত থাকত। এই ধরনের সভ্যতার শুরু গ্রিকরা করেননি, করেছিলেন ফিনিকীয়রা। তুর (Tyre), সিদন (Sidan) ও কার্থেজ অভ্যন্তরীণ শারীরিক পরিশ্রমের জন্য নির্ভর করত ক্রীতদাসদের উপর এবং যুদ্ধের জন্য নির্ভর করত বেতনভুক সৈন্যদের উপর।
আধুনিক রাজনীতিগুলোর মতো একই জাতি এবং সমান রাজনৈতিক অধিকারসম্পন্ন বিরাট গ্রামীণ জনতার উপর নির্ভর করত না। আধুনিককালে এর সঙ্গে নিকটতম সাদৃশ্য দেখা যায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের দূরপ্রাচ্যে। সিঙ্গাপুর ও হংকং, শাংহাই ও চীনের অন্যান্য সন্ধি বন্দরগুলো ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইয়োরোপীয় দ্বীপ, সেখানে কুলিদের শ্রমের উপর নির্ভরশীল শ্বেতকায়রা ছিলেন বণিক অভিজাত। উত্তর আমেরিকাতে, মেসন-ডিক্সন লাইনের উত্তরে সেরকম শ্রমিক অমিল হওয়ায় শ্বেতকায়রা কৃষিকাজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই কারণে উত্তর আমেরিকার উপর শ্বেতকায়দের আধিপত্য নিরাপদ কিন্তু দূরপ্রাচ্যে তাঁদের অধিকার ইতোমধ্যেই অনেক হ্রাস পেয়েছে এবং সহজেই বিলুপ্ত হওয়া সম্ভব। এই ধরনের সংস্কৃতির বহুলাংশ, বিশেষ করে শিল্পসভ্যতা কিন্তু বেঁচে থাকবে। এই সাদৃশ্য আমাদের আলেকজান্দ্রসের সম্রাজ্যের পূর্বদিকের গ্রিকদের অবস্থা বুঝতে সাহায্য করবে।
এশিয়ার কল্পলোকে আলেকজান্দ্রসের প্রভাব ছিল বিরাট ও দীর্ঘস্থায়ী। ফার্স্ট বুক অ দি ম্যাকাৰীজ (First Book of Maccabees) গ্রন্থটি আলেকজান্দ্রসের মৃত্যুর বহু শতাব্দী পর রচিত, শুরু হয়েছে তার কর্মজীবনের ইতিহাস দিয়ে।
এবং এরকম ঘটেছিল যে, খেত্তিম (Chettim)-এর দেশ থেকে আগত মাকেদনীয় ফিলিপের ছেলে আলেকজান্দ্রসের দ্বারা পারস্য ও মেদেস-এর রাজা দারিয়সকে পরাজিত করার পর, তাঁর স্থানে আলেকজান্দ্রসই রাজত্ব করেন। তিনি প্রথমে রাজত্ব করেন গ্রিসে এবং অনেক যুদ্ধ করেন ও অনেক শত্রুঘাঁটি দখল করেন, তিনি পৃথিবীর রাজাদের নিহত করেন ও পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। তিনি বহু জাতিকে লুণ্ঠন করেছিলেন, ব্যাপারটা এমনই যে, তাঁর সামনে পৃথিবী নীরব হলো। তারপর তিনি মহিমান্বিত হলেন এবং তাঁর হৃদয় উচ্চে প্রতিষ্ঠিত হলো। এক মহাশক্তিশালী সৈন্যদল তিনি সংগ্রহ করেছিলেন এবং রাজত্ব করেছিলেন নানা দেশ, নানা জাতি ও রাজাদের উপর আর সেই রাজারা হয়েছিলেন তাঁর করদ রাজা। তারপর তিনি অসুস্থ হলেন এবং বুঝতে পারলেন তাঁর মৃত্যু নিকটে। তখন তিনি তাঁর ভৃত্যদের ডাকলেন। ডাকলেন সেই ভৃত্যদের যারা ঈমানদার এবং তরুণ বয়স থেকে তাঁর সঙ্গে বড় হয়েছেন। তারপর জীবিত অবস্থায় নিজের সাম্রাজ্য তাদের ভিতর ভাগ করে দিলেন। এইভাবে আলেকজান্দ্রস রাজত্ব করেছিলেন বারো বছর এবং তারপর তাঁর মুত্যু হয়েছিল।
আলেকজান্দ্রস মহম্মদীয় ধর্মে এক প্রবাদপ্রতিম বীররূপে বেঁচে রইলেন এবং এখনও হিমালয়ের অনেক ছোট ছোট সর্দার নিজেদের আলেকজান্দ্রসের বংশধররূপে দাবি করেন। এর আগে সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক কোনো বীর এই রকম প্রবাদ পুরুষ হওয়ার নিখুঁত সুযোগ গুছিয়ে রেখে যাননি।
আলেকজান্দ্রসের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ রাখার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর দুই পুত্রের একজন ছিল শিশু আর অন্যজনের তখনও জন্ম হয়নি। দুজনেরই সমর্থক ছিল কিন্তু তার ফলে যে গৃহযুদ্ধ হয়েছিল তাতে দুজনকেই সরিয়ে দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত আলেকজান্দ্রসের সাম্রাজ্য তাঁর তিন সেনাপতিদের মধ্যে ভাগ হয়, মোটামুটি বলা যায় তাঁদের ভিতর একজন পেয়েছিলেন ইউরোপীয় অংশ, একজন আফ্রিকায় অবস্থিত অংশ ও আর একজন পেয়েছিলেন তাঁর সাম্রাজ্যের এশিয়ায় অবস্থিত অংশ। ইয়োরোপীয় অংশ শেষ পর্যন্ত পেয়েছিলেন আন্তিগনস (Antigones)- এর বংশধরেরা; মিশর পড়েছিল টলেমির ভাগে, তিনি তার রাজধানী করেছিলেন আলেকজান্দ্রিয়াতে। অনেক যুদ্ধের পর সেলুকস পেয়েছিলেন এশিয়া কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে খুবই ব্যস্ত থাকাতে সুস্থিত কোনো রাজধানী তিনি করতে পারেননি তবে পরবর্তী যুগে আন্তিয়খ (Antioch) ছিল তাঁর বংশের প্রধান নগরী।
টলেমীয় ও সেলুকিডরা (সেলুকসের বংশধরেরা এই নামেই পরিচিত ছিলেন) উভয়েই আলেকজান্দ্রসের গ্রিক ও বর্বরদের সংযুক্তির প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করেন এবং সামরিক স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে এর ভিত্তি ছিল গ্রিক পেশাদার সৈনিকদের সাহায্যে বর্ধিতশক্তি মাকেদনীয় সৈন্যবাহিনীর নিজ নিজ অংশ। টলেমীয়রা বেশ শক্ত করেই মিশরকে ধরে রেখেছিলেন কিন্তু এশিয়াতে দুই শতাব্দীব্যাপী গোলমেলে রাজবংশভিত্তিক যুদ্ধ শেষ হয় রোমকদের বিজয়ের পর। এই শতাব্দীগুলোতে পারস্য জয় করেন পার্থিয়ানরা এবং ব্যাকট্রীয় গ্রিকরা অধিকতর বিচ্ছিন্ন হয়ে যান।
খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে (তারপর তাঁদের দ্রুত অধঃপতন হয়) মিনান্দ্রস (Menander) নামে তাদের একজন রাজার ভারতে বিস্তৃত এক সাম্রাজ্য ছিল। তার সঙ্গে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর কথোপকথন পালিভাষায় রয়ে গিয়েছে এবং একটি চীনা অনুবাদেও অংশত আছে। ড. টার্ন (Tran)-এর ইঙ্গিত- এগুলোর প্রথমটির ভিত্তি মূল গ্রিকে, দ্বিতীয়টির শেষে নিমান্দ্রস রাজ্য ত্যাগ করে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হয়ে যান, এর মূল নিশ্চয়ই গ্রিক ভাষায় নয়।
সেই সময় বৌদ্ধধর্ম, ধর্মান্তরকরণে অভ্যস্ত একটি সতেজ ধর্ম ছিল। ঋষিতুল্য বৌদ্ধ রাজা অশোখ (২৬৪-২২৮) এর এখনও বর্তমান একটি শিলালিপিতে খোদিত আছে যে, তিনি সমস্ত মাকেদনীয় রাজাদের কাছে প্রচারক পাঠিয়েছিলেনঃ এবং মহারাজের মতে এটাই তার প্রধানতম বিজয় অর্থাৎ নীতির দ্বারা জয়। মহারাজ এই বিজয় অভিযান করেছেন নিজের রাজ্যে এবং ছয় শত লিগ (league- প্রায় সাড়ে তিন মাইল) দূরত্ব পর্যন্ত সমস্ত প্রতিবেশী রাজ্যে- এমনকি, যেখানে গ্রিক রাজা আন্তিওখস (Antiochus) থাকেন সেই পর্যন্ত এবং সেই আন্তিওখসের এবং আলেকজান্দ্রস…… এবং এখানেও, রাজার রাজত্বে, যবনদের ভিতরে (অর্থাৎ পাঞ্জাবের গ্রিকদের ভিতরে)। দুর্ভাগ্যক্রমে এই ধর্মদূতদের কোনো পাশ্চাত্য ইতিহাস পাওয়া যায়নি।
ব্যাবিলনিয়ায় হেলেনীয় প্রভাব আরও অনেক গভীর ছিল। আমরা যেমন দেখেছি সামস-এর আরিস্তারখসের প্রকল্পিত কোপারনিকাসীয় তন্ত্র প্রাচীনকালে একজনই অনুসরণ করেছিলেন, তিনি হলেন টাইগ্রিস-এর তীরে অবস্থিত সেলুকিয়া-র সেলুকস। তাঁর জীবনকাল খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০-এর কাছাকাছি। তাকিতস (Tacitus) আমাদের বলছেন, প্রথম শতাব্দীতে সেলুকিয়া পার্থিয়ানদের বর্বর আচার ব্যবহারে প্রত্যাবর্তন করেনি এবং তখনও গ্রিক প্রতিষ্ঠাতা সেলুকসের প্রতিষ্ঠানগুলো রক্ষা করছিল। অর্থ কিংবা প্রজ্ঞার ভিত্তিতে তিন শত নাগরিককে বেছে নেওয়া হতো, তাঁরা সেনেট-এর মতো একটা কিছু গঠন করতেন, জনসাধারণও ক্ষমতার অংশীদার হতেন।১২ সমগ্র মেসোপটেমিয়ায় ও আরও পশ্চিমে গ্রিকই ছিল সাহিত্য এবং সংস্কৃতির ভাষা এবং মহম্মদীয় বিজয় পর্যন্ত সেই অবস্থাই ছিল।
সিরিয়ার নগরগুলো (জুডিয়া বাদে) ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে হেলেনীয় হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু গ্রামীণ মানুষ ছিল বেশি রক্ষণশীল, যে ধর্ম ভাষায় তারা অভ্যস্ত সেগুলো তারা বজায় রেখেছিল।১৩ এশিয়া মাইনরে সমুদ্র তীরের গ্রিক নগরগুলোর প্রভাব তাদের বর্বর প্রতিবেশীদের উপর ছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী। মাকেদনীয় বিজয়ের পর এই প্রভাব আরও গম্ভীর হয়েছিল। ইহুদিদের সঙ্গে গ্রিকদের প্রথম সংঘাতের কথা লেখা আছে বুকস অব দি ম্যাকাবীজ-এ। গভীর কৌতূহলোদ্দীপক এই কাহিনি, মাকেদনীয় সাম্রাজ্যের অন্য সবকিছুর থেকে আলাদা। পরে যখন খ্রিষ্টধর্মের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির কাহিনিতে আসব তখন এ নিয়ে আলোচনা করব। অন্য কোথাও গ্রিক প্রভাব এমন কঠোর বিরোধিতার সম্মুখীন হয়নি।
হেলেনীয় সংস্কৃতির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সাফল্য হলো আলেকজান্দ্রিয়া নগরী। মাকেদনীয় সাম্রাজ্যের ইয়োরোপ ও এশিয়ার অংশগুলোর তুলনায় মিশরে যুদ্ধের আশঙ্কা অল্প ছিল এবং বাণিজ্যের দিক থেকে আলেকজান্দ্রিয়ার অবস্থান ছিল অসাধারণ সুবিধাজনক। টলেমীয়রা বিদ্যার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁদের রাজধানীতে সে যুগের শ্রেষ্ঠ পুরুষদের আকর্ষণ করেছিলেন। গণিতশাস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রধানত আলেকজান্দ্রীয় এবং রোমের পতনের পূর্ব পর্যন্ত এই অবস্থা বজায় ছিল। একথা সত্য, আর্থিমিদেস ছিলেন সিসিলীয় এবং তিনি পৃথিবীর সেই অংশের অধিবাসী ছিলেন যেখানে গ্রিক নগররাষ্ট্রগুলো তাদের স্বাধীনতা বজায় রেখেছিলেন (খ্রিষ্টপূর্ব ২১৩-তে তাঁর মৃত্যু মুহূর্ত পর্যন্ত)। কিন্তু তিনিও আলেকজান্দ্রিয়াতে লেখাপড়া শিখেছিলেন। আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত গ্রন্থাগারের প্রধান গ্রন্থাগারিক ছিলেন এরাতোস্থেনেস (Eratosthenes)। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে আলেকজান্দ্রিয়ার সঙ্গে কমবেশি সম্পর্কিত গণিতবিদ ও বৈজ্ঞানিকরা পূর্ব শতাব্দীর গ্রিকদের মতোই পটু ছিলেন এবং একই রকম গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। কিন্তু তাঁদের পূর্বগামীদের মতো তাঁরা সমস্ত জ্ঞানকেই নিজের এলাকা মনে করে বিশ্বজনীন দর্শন উপস্থিত করতেন না, আধুনিক অর্থে তাঁরা ছিলেন বিশেষজ্ঞ। এউক্লিদ, আরিস্তাখস, আর্থিমিদেস এবং আপল্লনিয়স গণিতবিদ হয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন, দর্শনশাস্ত্রে মৌলিকত্বের কোনো আকাক্ষা তাদের ছিল না।
এই যুগে বিশেষজ্ঞতা শুধুমাত্র পাণ্ডিত্যের জগতেরই নয়, সমস্ত বিভাগেরই বৈশিষ্ট্য। পঞ্চম ও চতুর্থই শতাব্দীর স্বশাসিত গ্রিক নগরগুলোতে একজন সক্ষম পুরুষকে সর্ব বিষয়ের সক্ষম বলে অনুমান করা হতো। অবস্থার দাবির সঙ্গে তাকে সৈন্য, রাজনীতিবিদ, আইনপ্রণেতা কিংবা দার্শনিক হতে হতো। সক্রাতেস যদিও রাজনীতি অপছন্দ করতেন তবুও তিনি রাজনীতির দ্বন্দ্বে জড়ানো এড়াতে পারেনি। যৌবনে তিনি সৈন্য ছিলেন এবং (অ্যাপলজি বইতে অস্বীকৃতি থাকলেও) ভৌতবিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। প্রতাগরস যখন আধুনিকতম বস্তুর সন্ধানী অভিজাত তরুণদের সন্দেহবাদ শিক্ষা দিয়ে সময় পেতেন তখন থুরি-র জন্য আইনের সংকলন গ্রন্থ প্রণয়ন করতেন। প্লাতন শখের রাজনীতি করতেন, যদিও অসফলভাবে। জেনোফন যখন সাতেসের জীবনী লিখতেন না কিংবা গ্রামীণ ভদ্রজনোচিত জীবনযাপন করতেন
তখন তার অতিরিক্ত সময়ে সেনাপতির কাজ করতেন। পুথাগোরীয় গণিতবিদরা চেষ্টা করেছিলেন নগরগুলোর শাসক হতে। প্রত্যেককেই জুরির কাজ করতে হতো এবং জনসাধারণের জন্য নানা কর্তব্য কর্ম করতে হতো। তৃতীয় শতকে এ সবেরই পরিবর্তন হলো। প্রাচীন নগররাষ্ট্রে রাজনীতি চালু ছিল একথা সত্য কিন্তু সে রাজনীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল সংকীর্ণ ও গুরুত্বহীন। কারণ, তখন গ্রিস ছিল মাকেদনীয় সৈন্যদের করুণানির্ভর। ক্ষমতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ দ্বন্দ্ব ছিল মাকেদনীয় সৈন্যদের ভিতরে, সে দ্বন্দ্বের সঙ্গে নীতির কোনো প্রশ্ন জড়িত থাকত না, থাকত শুধুমাত্র দুঃসাহসিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের ভিতরে বিভিন্ন অঞ্চলের ভাগ নিয়ে দ্বন্দ্ব। প্রশাসন এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এই স্বল্পাধিক অশিক্ষিত সৈন্যরা গ্রিকদের নিয়োগ করতে বিশেষজ্ঞরূপে, উদাহরণ-মিশরে সেচ ও নিকাশি ব্যবস্থার জন্য অতি উস্কৃষ্ট কাজ হয়েছিল। সৈন্য, প্রশাসক, চিকিৎসক, গণিতবিদ, দার্শনিক ছিলেন কিন্তু একাধারে সবই জানেন এরকম কোনো ব্যক্তি ছিলেন না।
যুগটা এমন ছিল যে অর্থবান কিন্তু ক্ষমতার আকাক্ষী নয়, সে বেশ আনন্দময় জীবন কাটাতে পারত সবসময় একথা ভেবে নিয়ে যে, কোনো লুঠেরা সৈন্যবাহিনী তাকে বাধা দিতে আসবে না। পণ্ডিত মানুষ কোনো রাজার প্রিয়পাত্র এবং দক্ষ স্তাবক হতে পারলে ও অশিক্ষিত রাজার রসিকতার লক্ষ্য হতে আপত্তি না করলে বেশ উচ্চ মানের বিলাস ভোগ করতে পারতেন। কিন্তু নিরাপত্তা নামক কোনো কিছু ছিল না। প্রাসাদ বিপ্লবে স্তাবক ঋষির পৃষ্ঠপোষক স্থানচ্যুত হতে পারত। গ্যালাতীয়রা [Galatians-এশিয়া মাইনরে অবস্থিত একটি দেশের অধিবাসী, অনেকে মনে করেন খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে গ্যালাত (Galat) দেশ জয় করে গ্যালাতীয়রা সেখানের অভিবাসী হন-অনুবাদক] ধনীর বিলাসভবন ধ্বংস করতে পারত, রাজবংশের অন্তর্দ্বন্দ্বের এক ঘটনায় নিজেদের শহর ধ্বংস হতে পারত। এইরকম পরিস্থিতিতে মানুষ যে ভাগ্যদেবীর কিংবা সৌভাগ্যদেবীর পূজা করবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। মানবিক পরিস্থিতির চালচলনে যুক্তিসিদ্ধ কিছু ছিল না বলেই মনে করা হতো। যারা একগুয়ের মতো কোথাও না কোথাও যুক্তি খুঁজতেন তারা আত্মসমাহিত হয়ে থাকতেন এবং মিলটনের শয়তানের মতো সিদ্ধান্ত করতেন, যে
মনই তার নিজস্ব স্থান এবং নিজের ভিতরেই।
পারে নরককে স্বর্গ এবং স্বৰ্গকে নরক করতে।
শুধুমাত্র দুঃসাহসী স্বার্থান্বেষী ছাড়া এ অবস্থায় জনস্বার্থে আর উদ্যোগ নেওয়ার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। আলেকজান্দ্রসের চমঙ্কার বিজয় অভিযান পর্বের পর স্থায়ী প্রাধান্য অর্জন করার যোগ্য একজন স্বৈরতন্ত্রীর অভাবে কিংবা সামাজিক সংযুক্তি সাধনে সক্ষম শক্তিশালী নীতির অভাবে হেলেনীয় জগৎ বিশৃঙ্খলায় ডুবে যাচ্ছিল। নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে গ্রিক বুদ্ধিমত্তা পরিপূর্ণ অযোগ্যতা প্রদর্শন করল। নিঃসন্দেহে গ্রিকদের তুলনায় রোমকরা ছিলেন বোকা ও পাশবিক কিন্তু অন্ততপক্ষে তাঁরা শৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। স্বাধীন যুগের অতীত বিশৃঙ্খলা সহ্য করা যেত, কারণ, প্রতিটি নাগরিকেরই এই বিশৃঙ্খলায় অংশ ছিল কিন্তু অযোগ্য শাসকদের প্রজাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া মাকেদনীয় বিশৃঙ্খলা ছিল একেবারেই অসহনীয় পরবর্তীকালে রোমের অধীনতার চাইতেও বেশি অসহনীয় ছিল।
সমাজে অসন্তোষ ছিল ব্যাপক এবং ছিল বিপ্লবের ভয়। স্বাধীন মজুরদের মজুরি হ্রাস পেল, যতদূর সম্ভব এর কারণ ছিল পূর্বদেশের দাস শ্রমিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা এবং এর ভিতরে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি হলো। দেখা যায়, আলেকজান্দ্রস তাঁর কর্মজীবনের শুরুতে গরিবদের যথাস্থানে রাখবার জন্য সন্ধি করার সময় পাচ্ছেন। ৩৬৫ খ্রিষ্টাব্দে আলেকজান্দ্রস এবং কোরিন্থের রাষ্ট্রসংঘের ভিতরে কৃত সন্ধিতে ব্যবস্থা ছিল রাষ্ট্রসংঘের কাউন্সিল ও আলেকজান্দ্রসের প্রতিনিধিরা নজর রাখবেন যাতে রাষ্ট্রসংঘের কোনো নগরেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত না হয় কিংবা জমি ভাগ করা, কিংবা ঋণ নাকচ করা কিংবা বিপ্লবের উদ্দেশ্যে ক্রীতদাসদের মুক্তি না দেওয়া হয়।১০৪ হেলেনায়িত জগতে মন্দিরগুলো ছিল ব্যাঙ্ক, তারা ছিল সঞ্চিত সোনার মালিক এবং ঋণদান নিয়ন্ত্রণ করত তারা। তৃতীয় শতকের প্রথম দিকে দেলস-এ অ্যাপোলোর মন্দির দশ শতাংশ হারে সুদে টাকা ধার দিত, তার আগে সুদের হার ছিল আরও বেশি।
স্বাধীন শ্রমিকরা, এমনকি অবশ্য প্রয়োজনীয়ের জন্যও মজুরি অপ্রতুল হলে, ভাড়াটে সৈন্যের চাকরি পেতে পারত। অবশ্য তরুণ ও স্বাস্থ্যবান হলে। সন্দেহ নেই, ভাড়াটে সৈন্যের জীবন কঠিন এবং বিপজ্জনক কিন্তু তা হলেও ছিল বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ। পূর্বদেশের কোনো সমৃদ্ধ নগর লুণ্ঠন করার সম্ভাবনা আসতে পারত, হয়তো বা লাভজনক বিদ্রোহের সম্ভাবনা থাকত। একজন সেনানায়কের নিজের সৈন্যদল ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা অবশ্যই বিপজ্জনক ছিল এবং অবিচ্ছিন্ন যুদ্ধবিগ্রহের এটাও নিশ্চয়ই একটা কারণ ছিল।
প্রাচীন নাগরিক চেতনা প্রাচীন গ্রিক নগরগুলোতে কমবেশি জীবিত ছিল কিন্তু আলেকজান্দ্রসের পত্তন করা নতুন নগরীগুলোতে ছিল না-এমনকি হতো পুরোনো একটি নগর থেকে আসা অভিবাসীদের উপনিবেশ এবং নতুন নগর তার জন্মদাতা নগরের সঙ্গে আবেগের বন্ধনে সংযুক্ত থাকত। এই জাতীয় আবেগ খুবই দীর্ঘায়ু হতো, উদাহরণ, এটা দেখা যায় ১৯৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে হেলেস্পন্ত-এ ল্যাম্পসাকস (Lampsacus) এর কূটনৈতিক ক্রিয়াকলাপে। সেলুকিড-এর রাজা তৃতীয় আন্তিওখস এই নগরকে নিজের অধীনে আনবার ভয় দেখিয়েছিলেন এবং তাঁরা আত্মরক্ষার জন্য রোমের সাহায্য প্রার্থনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। একদল রাষ্ট্রপ্রতিনিধি (embassy) পাঠানো হলো কিন্তু তারা সরাসরি রোমে গেলেন না, বিশাল দূরত্ব সত্ত্বেও তারা প্রথম গেলেন মার্সাই এ, সেটাও ল্যাম্পসাকসের মতো ফকায়েআ (Phocaea)-র উপনিবেশ ছিল এবং রোমকরাও তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখতেন। মাসাইয়ের নাগরিকরা প্রতিনিধিদলের বক্তৃতা শুনে তাঁদের সহোদরা নগরীকে সমর্থনের জন্য তৎক্ষণাৎ রোমে নিজস্ব কূটনৈতিক প্রতিনিধি পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। গলরা মার্সাইয়ের উপকূল থেকে ভিতরের দিকে থাকতেন, তাঁরা এশিয়া মাইনরে তাঁদের আত্মীয় গ্যালাতীয়দের একটা চিঠি দিয়ে ল্যাম্পসাকসের সঙ্গে তাদের বন্ধুত্বের সুপারিশ করেন। রোম স্বভাবতই এশিয়া মাইনরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার এই অজুহাত পেয়ে খুশি হয়েছিল এবং রোমের হস্তক্ষেপে ল্যাম্পসাকস রোমের অসুবিধা না হওয়া পর্যন্ত নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করে।
সাধারণভাবে এশিয়ার শাসকরা নিজেদের বলতেন ফিল-হেলেন (Phil Hellene-গ্রিসের সমর্থক-অনুবাদক) এবং তাঁরা নীতি ও সামরিক প্রয়োজনের অনুমোদন সাপেক্ষ প্রাচীন গ্রিক নগরগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতেন। নগরগুলোর ইচ্ছা থাকত এবং (যখন তারা পারত) নিজেদের অধিকাররূপে দাবি করত- গণতান্ত্রিক স্ব শাসন, করের অনস্তিত্ব ও রাজকীয় সেনানিবাস থেকে মুক্তি। তাদের শুভেচ্ছার প্রয়োজন। ছিল, কারণ, তারা ছিল ধনী, তারা ভাড়াটে সৈন্য যোগাতে পারত এবং তাদের অনেকেরই গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ছিল। কিন্তু গৃহযুদ্ধে তারা ভুল পক্ষে যোগ দিলে সরাসরি বিজিত হওয়ার আশঙ্কা থাকত। মোটের উপর সেলুকিড ও অন্যান্য রাজবংশগুলো-যারা ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠল, তারাও তাদের সঙ্গে সহনশীল ব্যবহার করত কিন্তু অনেক ব্যতিক্রমও ছিল।
নতুন নগরগুলোর কিছুটা স্বায়ত্তশাসন থাকলেও পুরোনো নগরগুলোর ঐতিহ্য তাদের ছিল না। তাদের নাগরিকরা সমজাত ছিলেন না, ছিলেন গ্রিসের সমস্ত অংশ থেকে আগত। প্রধানত তাঁরা ছিলেন বিজয়ী বীরদের (conquistadores- প্রধানত দক্ষিণ আমেরিকার স্পেনীয় লুঠেরা ও যুদ্ধবাজ) মতো ভাগ্যান্বেষী কিংবা জোহানেসবার্গের অভিবাসীদের মতো আগেকার গ্রিক অভিবাসীদের মতো কিংবা নিউ ইংল্যান্ডের নব্য প্রবর্তকদের মতো ধার্মিক তীর্থযাত্রী নয়। ফলে আলেকজান্দ্রসের কোনো নগরই শক্তিশালী রাজনৈতিক এককরূপে গড়ে ওঠেনি। রাজার সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাপারটা সুবিধাজনক ছিল কিন্তু হেলেনীয় সভ্যতা প্রসারের দিক থেকে এ ছিল একটা দুর্বলতা।
হেলেনায়িত জগতের উপর অ-গ্রিক ধর্ম ও কুসংস্কারের প্রভাব প্রধানত ছিল মন্দ কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নয়। ব্যাপারটা এরকম নাও হতে পারত। ইহুদি, পারসিক ও বৌদ্ধ এঁদের প্রত্যেকের ধর্মই ছিল সাধারণ গ্রিকদের বহু দেবতা পূজার চাইতে অতি নিশ্চিতভাবে উন্নত এবং এগুলো পাঠ করলে শ্রেষ্ঠ দার্শনিকরাও লাভবান হতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ব্যাবিলনীয় কিংবা খালদীয়রা গ্রিক কল্পনাকে সবচাইতে বেশি প্রভাবিত করেছিল। প্রথমত তাদের ছিল এক উপকথার মতো প্রাচীনত্ব, পুরোহিতদের নথিপত্র ছিল হাজার হাজার বছরের পুরোনো এবং ঘোষণা করতেন তাঁদের প্রাচীনত্ব আরও বহু সহস্র বছরের। তাঁদের ছিল কিছু সত্যকার প্রজ্ঞাঃ ব্যাবিলনীয়রা গ্রিকদের অনেক আগেই গ্রহণ সম্পর্কে কমবেশি ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারতেন। তবে এগুলো শুধুমাত্র প্রভাবিত হওয়ার কারণ, যা তারা গ্রহণ করেছিলেন সেগুলো প্রধানত ছিল জ্যোতিষশাস্ত্র ও জাদুবিদ্যা। অধ্যাপক গিলবার্ট মারে বলেন, হেলেনায়িত মানুষের উপর জ্যোতিশাস্ত্রের আক্রমণ ছিল একটি প্রত্যন্ত দ্বীপের মানুষের উপর নতুন একটি ব্যাধির আক্রমণের মতো। দিওদরস-এর বিবরণ অনুসারে ওজিমানদিয়াস (Ozymandias)-এর কবর ঢাকা ছিল জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতীক ও সঙ্কেত দিয়ে এবং কম্মাজেন (Commagene)-এ আবিষ্কৃত প্রথম আন্তিওখস-এর কবরও একইরকম চরিত্রের। তারকারা তাঁদের উপর নজর রাখছে এরকম ভাবা রাজাদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু আপামর জনসাধারণ ছিলেন এই জীবাণু গ্রহণ করতে প্রস্তুত।০৭ মনে হয় জ্যোতিষশাস্ত্র আলেকজান্দ্রসের আমলেই প্রথম গ্রিকদের শেখান বেরসস (Berosus) নামে একজন খালদীয়, তিনি পড়াতেন কস (Cos)-এ এবং সেনেকা-র বিবরণ অনুসারে তিনি বেল ব্যাখ্যা করতেন। অধ্যাপক মারে-র মতে এর অর্থ নিশ্চয়ই ছিল গ্রিক ভাষায় তিনি আই অব বেল অনুবাদ করেছেন, সত্তরটি ফলকে লেখা এই বইটি পাওয়া গিয়েছিল আসুর বাণী-পাল (Assur-bani-pal)-এর গ্রন্থাগারে (৬৮৬-৬২৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) কিন্তু এটা লেখা হয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দে প্রথম সারগন-এর জন্য। (তদেব, পৃষ্ঠা-১৭৬ দ্রষ্টব্য)।
আমরা দেখতে পাব অধিকাংশই, এমনকি শ্রেষ্ঠ দার্শনিকরাও জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিলেন। যেহেতু জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান সম্ভব সেহেতু এর সঙ্গে জড়িত ছিল প্রয়োজন কিংবা নিয়তিতে বিশ্বাস। এই বিশ্বাসকে তখনকার প্রচলিত অদৃষ্ট (fortune) সম্পৰ্কীয় বিশ্বাসের বিপরীতে স্থাপন করা সম্ভব। হয়েছিল। সন্দেহ নেই, অধিকাংশের বিশ্বাস ছিল দুটোতেই এবং এ দুটোর ভিতরে অসঙ্গতি কোনোদিনই নজরে পড়েনি।
সাধারণ বিশৃঙ্খলা বৌদ্ধিক দুর্বলতার চাইতেও অবশ্যম্ভাবীরূপে নিয়ে এল নৈতিক অবক্ষয়। বহুযুগব্যাপী অনিশ্চয়তার সময়ের সঙ্গে হয়তো মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সর্বোচ্চ ঋষিতুল্য ভাবের সঙ্গতি থাকতে পারে কিন্তু সেটা ছিল সম্ভ্রান্ত নাগরিকদের দৈনন্দিন গদ্যময় জীবনে সদগুণের বিরোধী। আগামীকাল যদি আপনার সমস্ত সঞ্চয় নষ্ট হয়ে যায় তাহলে মিতব্যয়িতার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। সৎ ব্যবহার প্রাপ্ত মানুষ আপনাকে ঠকাবে এটা যদি নিশ্চিত হয় তাহলে সততায় কোনো সুবিধা থাকে না। যখন কোনো উদ্দেশ্যেরই গুরুত্ব নেই কিংবা স্থায়ী বিজয়ের সম্ভাবনা নেই তখন কোনো উদ্দেশ্যের প্রতি স্থির আনুগত্যে কী লাভ? যখন নমনীয়ভাবে সহজ মত পরিবর্তনেই শুধুমাত্র জীবনরক্ষা ও সম্পদ রক্ষা সম্ভব তখন সত্যবাদিতার সপক্ষে কোনো যুক্তি থাকে না। পার্থিব বিচক্ষণতা ছাড়া যার সদগুণের কোনো উৎস নেই-এ রকম পরিস্থিতিতে সাহস থাকলে সে হবে দুঃসাহসী অভিযাত্রী, না থাকলে সে কর্তাভজা (time-server) হয়ে একটা অখ্যাত জীবন খুঁজবে।
মিনান্দ্রস ছিলেন এই যুগেরই লোক, তিনি বলছেঃ
কত ঘটনাই আমি দেখেছি।
যদিও স্বভাবে তারা দুবৃত্ত নয়,
তবুও তারা দুবৃত্ত হয়েছে-দুর্ভাগ্যে ও দুর্ভোগে।
এটাই মনে হয় খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের নৈতিক চরিত্রের সংক্ষিপ্ত সার- ব্যতিক্রম শুধু কয়েকজন ব্যতিক্রমী মানুষ। এমনকি, এই কজন মুষ্টিমেয় লোকের ভিতরেও আশার স্থান দখল করেছিল ভীতি, জীবনের উদ্দেশ্য ছিল দুর্ভাগ্যকে এড়ানো উদ্দেশ্য ছিল না কোনো নিশ্চিত সুকর্ম করা। অধিবিদ্যা পশ্চাৎপটে অদৃশ্য হয় এবং নীতিশাস্ত্র হয়ে দাঁড়ায় ব্যক্তিগত ও সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। দর্শনশাস্ত্র তখন আর কয়েকজন দুঃসাহসী সত্যসন্ধানীর সম্মুখবর্তী অগ্নিস্তম্ভ নয় : এ যেন জীবন-সংগ্রামের পায়ে পায়ে চলা একটা রোগীবাহী শকট এবং তুলে নিচ্ছে দুর্বল ও আহতদের।