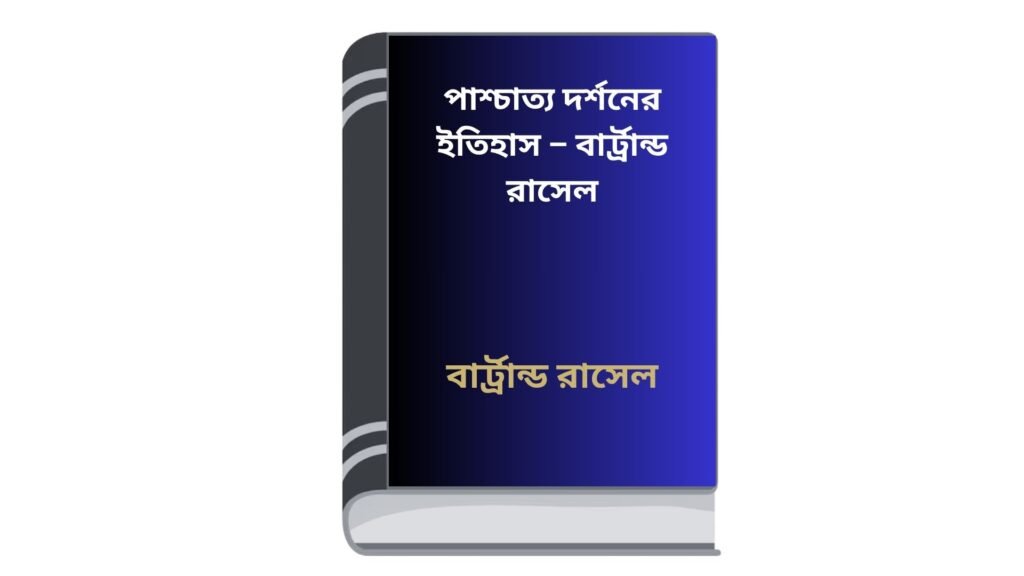২৭. এপিকুরীয় যুগ
২৭. এপিকুরীয় যুগ
স্টোইক ও এপিকুরীয়রা হেলেনায়িত যুগের নতুন দুই বিরাট দার্শনিক সম্প্রদায়-যারা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দিক থেকে সমসাময়িক। তাদের প্রতিষ্ঠাতা জেনো (Zeno) এবং এপিকুরস (Epicurus)-এর জন্ম হয়েছিল প্রায় একই সময়ে এবং তাঁদের নিজ সম্প্রদায়ের নেতারূপে আথিনাতে বসবাস শুরু করেন কয়েক বছর আগে পরে। সুতরাং কোনটা দিয়ে শুরু করব সেটা রুচির ব্যাপার। আমি শুরু করব এপিকুরীয়দের নিয়ে, কারণ, তাঁদের মতবাদগুলো প্রতিষ্ঠাতার দ্বারা চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট ছিল কিন্তু স্টোইকবাদের ছিল দীর্ঘ বিকাশকাল, এর বিস্তৃতি ছিল সম্রাট মার্ক অরেলিয়স (Marcus Aurelius) পর্যন্ত, এই সম্রাটের মৃত্যু হয় ১৮০ খ্রিষ্টাব্দে।
এপিকুরস সম্পর্কে প্রধান প্রামাণ্য বক্তা দিঅগেনেস লারতিয়স, (Diogenes Laertius), তাঁর জীবনকাল খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী। কিন্তু দুটি অসুবিধা আছে: প্রথমে যেসব কাহিনিগুলোর ঐতিহাসিক মূল্য সামান্য অথবা শূন্য, দিঅগেনেস লারতিয়স নিজেই সেগুলো মেনে নিতে রাজি। দ্বিতীয়, তাঁর জীবন নামক পুস্তকের একটা অংশে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে স্টোইকবাদের দ্বারা আনীত এপিকুরসের বিরুদ্ধে কলঙ্কজনক অভিযোগ এবং তিনি নিজে জোর করে কিছু বলেছেন নাকি শুধুমাত্র একটা লিখিত কুৎসা উল্লেখ করছেন- সেটা সব সময়ই স্পষ্ট নয়। স্টোইকদের দ্বারা আবিষ্কৃত কলঙ্কগুলো তাদের সম্পর্কে ঘটনা, তাঁদের উচ্চ নৈতিকতা প্রশংসিত হওয়ার সময় সেগুলো মনে রাখা উচিত কিন্তু এপিকুরস সম্পর্কে সেগুলো ঘটনা নয়। উদাহরণ, কথিত আছে তার মা ছিলেন একজন হাতুরে পুরোহিত, এ সম্পর্কে দিঅগেনেস বলেছেন :
তারা (দৃশ্যত স্টোইকরা) বলেন, তিনি মার সঙ্গে বাড়ি বাড়ি গিয়ে শুদ্ধিকরণ প্রার্থনা পাঠ করতেন ও সামান্য অর্থের বিনিময়ে তার বাবাকে প্রাথমিক শিক্ষাদানের কাজে সাহায্য করতেন।
এ সম্পর্কে বেইলি-এর মন্তব্যঃ তিনি তাঁর মার সঙ্গে অ্যাকোলাইট (acolyte গির্জার অধস্তন কর্মচারী) রূপে, বিধিমতো মন্ত্রোচ্চারণ করে ঘুরতেন- এ কাহিনিতে যদি সত্যতা থাকে তাহলে এটা সম্ভব যে, খুব অল্প বয়সেই তিনি কুসংস্কারকে ঘৃণা করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে সেটাই তাঁর দেওয়া শিক্ষার একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। এই তত্ত্ব আকর্ষণীয় কিন্তু প্রাচীন যুগের শেষাংশে কলঙ্ককাহিনি আবিষ্কারের ব্যাপারে চরম নীতিজ্ঞানহীনতার কথা মনে রাখলে এই তথ্যের কোনো ভিত্তি আছে বলে মেনে নেওয়া যায় না। এর বিরুদ্ধে এই তথ্য উপস্থিত করা যায়- মাকে তিনি অত্যন্ত গভীরভাবে ভালোবাসতেন, সচরাচর দেখা যায় না।
কিন্তু এপিকুরসের জীবন সম্পর্কে প্রধান তথ্যগুলো মনে হয় বেশ নিশ্চিত। তাঁর বাবা ছিলেন সামস-এর একজন দরিদ্র আথিনীয় অভিবাসী, এপিকুরসের জন্ম ৩৪২-১ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে কিন্তু তার জন্মস্থান সামস না আত্তিকা সেটা জানা নেই। সে যাই হোক, তাঁর বাল্যকাল কেটেছে সামস-এ। তিনি বলেছেন, চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি দর্শনশাস্ত্র পাঠ শুরু করেন। আঠারো বছর বয়সে প্রায় আলেকজান্দ্রসের মৃত্যুকালে তিনি আথিনাতে যান, মনে হয় তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নিজের নাগরিকত্ব প্রতিষ্ঠা করা কিন্তু সেখানে বাস করার সময় আথিনীয় অভিবাসীদের সামস থেকে বিতাড়িত করা হয় (৩২২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ)। এপিকুরসের পরিবার এশিয়া মাইনরে শরণার্থী হন, সেখানে এপিকুরস তাঁদের সঙ্গে পুনর্মিলিত হন। তাওস (Taos)-এ এই সময় কিংবা হয়তো কিছু আগে তিনি জনৈক নসিফানেস (Nausiphanes)-এর কাছে দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা নেন, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় নসিফানেস ছিলেন দেমক্রিতসের অনুগামী। যদিও তাঁর পরিণত দর্শন অন্য যে কোনো দার্শনিকের চাইতে বেশি ঋণী দেমক্রিতসের কাছে, তবুও তিনি নসিফানেস সম্পর্কে ঘৃণা ছাড়া অন্য কোনো ভাব প্রকাশ করেননি, সবসময় তাঁকে শম্বুকটা (The Molluse) বলে উল্লেখ করতেন।
৩১১ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে তিনি তাঁর বিদ্যালয় স্থাপন করেন, এটি প্রথমে ছিল মিতিলেনে (Mitylene)-তে, তারপর ল্যাম্পসাকস এ এবং ৩০৭ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে আথিনাতে, সেখানেই ২৭০-১ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে তার মৃত্যু ঘটে।
যৌবনের কঠিন সময়ের পর আথিনাতে তাঁর জীবনধারা ছিল শান্ত এবং একমাত্র অসুবিধা ছিল মন্দ স্বাস্থ্য। তাঁর একটি বাড়ি ও বাগান ছিল (আপাতদৃষ্টিতে বাড়ি ও বাগান ছিল পৃথক) এবং তিনি শিক্ষাদান করতেন বাগানে। তার তিন ভাই এবং আরও কয়েকজন শুরু থেকে বিদ্যালয়ের সদস্য ছিলেন কিন্তু আথিনাতে তাঁর গোষ্ঠী বেড়েছিল- শুধুমাত্র দর্শনশাস্ত্রের ছাত্ররাই নয়, ছিল বন্ধুবান্ধব ও তাদের ছেলেমেয়েরা, ক্রীতদাসরা ও রক্ষিতারা। শেষোক্ত জনরা তাঁর শত্রুদের রচিত কলঙ্কের বিষয়বস্তু ছিল, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অন্যায্যভাবে। বিশুদ্ধ মানবিক বন্ধুত্ব করার অতি অসাধারণ ক্ষমতা তাঁর ছিল এবং গোষ্ঠীর সদস্যদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের তিনি সুখপ্রদ চিঠি লিখতেন। আবেগ প্রকাশ করার ব্যাপারে প্রাচীন দার্শনিকদের মতো মর্যাদাপূর্ণ এবং সংযত ব্যবহারের চেষ্টা তিনি করতেন না, তাঁর চিঠিগুলো অদ্ভুতরকম স্বাভাবিক এবং ভান ও কৃত্রিমতাহীন।
গোষ্ঠীর জীবনযাত্রা ছিল খুবই সাদাসিধা, অংশত নীতির কারণে এবং অংশত (নিঃসন্দেহে) অর্থাভাবে। তাদের খাদ্য ও পানীয় ছিল রুটি আর জল, একে এপিকুরস খুবই সন্তোষজনক মনে করতেন। তিনি বলছেন, যখন আমি রুটি আর জল খেয়ে থাকি তখন দৈহিক আনন্দ আমাকে চমৎকৃত করে এবং বিলাসের আনন্দে আমি থুথু ফেলি, তার কারণ, সেই বিলাদ্রব্যগুলো নয়- তারা পরে যে অসুবিধা সৃষ্টি করে সেগুলোই তার কারণ, আর্থিক দিক দিয়ে গোষ্ঠীটি, অন্তত অংশত নির্ভর করত স্বেচ্ছাদানের উপর। তিনি লিখছেন, আমাকে কিছু সংরক্ষিত চীজ পাঠাবেন, আমার ইচ্ছা হলে আমি ভোজ খেতে পারি। আর একজন বন্ধুকেঃ তোমার নিজের এবং ছেলেমেয়ের পক্ষ থেকে আমাদের পবিত্র দেহ রক্ষার জন্য কিছু নৈবেদ্য পাঠাও। এবং পুনরায় ও একমাত্র যে সাহায্য আমি চাই সেটা হলো যে- শিষ্যদের আমার কাছে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন, এমনকি তারা উত্তরপ্রান্তবাসী হলেও। তোমাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে আমি চাই বার্ষিক দুইশত কুড়ি ড্রখমা, তার বেশি নয়।
এপিকুরস সারা জীবন ভুগেছেন মন্দ স্বাস্থ্যের জন্য কিন্তু অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করতে শিখেছিলেন। চরম বেদনাতেও মানুষ খুশি হতে পারে এ কথা তিনিই প্রথম বলেছিলেন, কোনো স্টোইক বলেননি। তাঁর লেখা দুটি চিঠি (একটি লেখা মৃত্যুর কয়েকদিন আগে, অপরটি মৃত্যু দিবসে লেখা) থেকে বোঝা যায় এরকম মতবাদ থাকার খানিকটা অধিকার তাঁর ছিল। প্রথম চিঠিতে আছেঃ এই চিঠি লেখার সাত দিন আগে বন্ধু হওয়া সম্পূর্ণ হয়েছিল এবং আমার এমনই ব্যথা হয়েছিল যে ব্যথা মানুষকে তার অন্তিমে নিয়ে যায়। আমার কিছু হলে মেত্রদরস (Metrodorus)-এর সন্তানদের চার কিংবা পাঁচ বছর দেখাশোনা কোরো কিন্তু আমার জন্য এখন তুমি যতটা ব্যয় কর, ওদের জন্য তার চাইতে বেশি ব্যয় কোরো না। দ্বিতীয় চিঠিতে আছেঃ এই আমার সত্যিকারের সুখের দিন, কারণ, এখন আমি মৃত্যুর মুখে তোমাকে চিঠি লিখছি। আমার মূত্রথলি পাকস্থলির ব্যাধি তাদের নিজ নিজ পথে চলেছে, তাদের সাধারণ তীব্রতার কোনো হানি হয়নি কিন্তু বিপরীত রয়েছে তোমার সঙ্গে বাক্যালাপের স্মৃতি, সেই স্মৃতি আমার অন্তরের আনন্দ। ছেলেবেলা থেকে আমার প্রতি এবং দর্শনশাস্ত্রের প্রতি তোমার অনুরাগের দাবিতে আমি আশা করতে পারি তুমি মেদরসে সন্তানদের ভালো করে যত্ন নেবে। মেত্রদরস ছিলেন তাঁর প্রথম শিষ্যদের একজন। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। এপিকুরস তাঁর উইল-এ এই শিষ্যের সন্তানদের ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন।
যদিও অধিকাংশ মানুষের প্রতি এপিকুরস ছিলেন ভদ্র ও দয়াশীল কিন্তু দার্শনিকদের সম্পর্কে বিশেষ করে যে সমস্ত দার্শনিকদের কাছে তিনি ঋণী ছিলেন বলে মনে হতে পারত, তাঁদের সম্পর্কে তাঁর চরিত্রের অন্য একটা দিক দেখা গিয়েছিল। তিনি বলছেন, আমার মনে হয় এইসব অসন্তুষ্ট লোকেরা বিশ্বাস করবেন আমি ছিলাম সেই শম্বুকটার (নসিফানেস) শিষ্য এবং কিছু মাতাল ছোকরার সঙ্গে তাঁর শিক্ষণ শুনেছি। কারণ, লোকটি ছিলেন সত্যিই মন্দ এবং তার অভ্যাস এমন ছিল কখনোই প্রজ্ঞার প্রতিকৃৎ হতে পারে না। তিনি কখনোই দেমক্রিতসের কাছে নিজের ঋণের পরিমাণ স্বীকার করেননি এবং লেউকিপ্পস সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঐ নামে কোনো দার্শনিক ছিলেন না। নিঃসন্দেহে তার অর্থ এই নয় যে, ঐ নামে কোনো মানুষ ছিলেন না- কিন্তু সে লোকটি দার্শনিক ছিলেন না। এপিকুরস তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিকদের সম্পর্কে যে সমস্ত অসম্মানজনক উপাধি প্রয়োগ করেছিলেন বলে মনে হয়, তার একটা পূর্ণ তালিকা দিয়েছেন দিঅগেনেস লারতিয়স। অন্যান্য দার্শনিকদের সম্পর্কে এই উদারতার অভাবের সঙ্গে তাঁর ছিল অপর একটি গুরুতর দোষ, সেটা হলো একনায়কসুলভ গোঁড়ামি। অনুগামীদের তাঁর মতবাদ দিয়ে গঠিত এক ধরনের নীতিশিক্ষা নিতে হতো যার সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করা অনুমোদিত ছিল না। শেষ পর্যন্ত তাদের কেউই সে মতবাদের কোনো পরিবর্তন অথবা পরিমার্জন করতে পারেননি। দই শতাব্দী পর লুক্ৰেতিয়স যখন এপিকুরসের দর্শনশাস্ত্রকে কবিতায় রূপান্তিত করেন তখন বিচার করে দেখা যায় তিনি তার গুরুর শিক্ষণে তাত্ত্বিক কিছু যোগ করেননি। যেখানে তুলনা সম্ভব সেখানেই দেখা যায় মূলের সঙ্গে লুক্রেতিয়সের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য রয়েছে এবং এ বিষয়ে সাধারণ মত- এপিকুরসের লেখা তিনশ বইয়ের সবগুলো হারিয়ে যাওয়ার ফলে জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল সেটা পূর্ণ করার জন্য অন্য জায়গায় তাঁকে ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে। তাঁর লেখার ভিতরে কয়েকটি চিঠি, কিছু টুকরো লেখা এবং প্রধান মতবাদ সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন ছাড়া কিছুই পাওয়া যায়নি।
মূলত তাঁর যুগের সকলের মতোই (সন্দেহবাদের আংশিক ব্যতিক্রম ছাড়া) এপিকুরসে দর্শনশাস্ত্র তৈরি হয়েছিল শান্তি পাওয়ার জন্য। তাঁর বিচারে আনন্দই একমাত্র উত্তম এবং এই দৃষ্টিভঙ্গির সমস্ত ফলের সঙ্গে তিনি লেগে থেকেছেন লক্ষণীয় সঙ্গতির সঙ্গে। তিনি বলেছেন, আনন্দই সুখী জীবনের শুরু ও শেষ। দিঅগেনেস লারতিয়স জীবনের শেষ (The End of Life) গ্রন্থে এপিকুরসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, আমি জানি না যদি স্বাদের আনন্দ, প্রেমের আনন্দ, দৃষ্টি ও শ্রুতির আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করি তাহলে উত্তমের ধারণা কী করে হবে, আবার সমস্ত উত্তমের শুরু এবং মূল রয়েছে পাকস্থলির আনন্দে, এমনকি প্রজ্ঞা ও সংস্কৃতির আনন্দকেও ঐদিকে আরোপ করতে হবে। বলা হয়েছে দৈহিক আনন্দের চিন্তনই মানসিক আনন্দ। দৈহিক আনন্দের তুলনায় এর একমাত্র সুবিধা- আমরা বেদনার চিন্তা না করে আনন্দের চিন্তা করা শিখতে পারি এবং এভাবে আমরা দৈহিক আনন্দের তুলনায় মানসিক আনন্দের উপর অধিক নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে পারি। সদগুণের অর্থ আনন্দের অনুসরণে বিচক্ষণতা, নাহলে এটা একটা শূন্যগর্ভ নাম। উদাহরণ, জীবনে সুবিচারের অর্থ এমনভাবে কাজ করা যাতে অপরের বিরাগ সৃষ্টির ভয় না থাকে। এই দৃষ্টিভঙ্গি সমাজের উৎপত্তি সম্পর্কিত একটি মতবাদের পথিকৃৎ, এর সঙ্গে সামাজিক চুক্তিতত্ত্বের সাদৃশ্য আছে।
সক্রিয় ও অক্রিয় আনন্দে কিংবা স্থিতীয় ও গতীয় আনন্দে পার্থক্যের ব্যাপারে ভোগবাদী পূর্বসূরিদের সঙ্গে এপিকুরসের পার্থক্য রয়েছে। গতীয় আনন্দ হলো ঈঙ্গিত লক্ষ্যপ্রাপ্তি, কারণ, প্রাক্তন ঈপ্সা ছিল বেদনার সঙ্গে জড়িত। স্থিতীয় আনন্দে রয়েছে এক ভারসাম্যের অবস্থা এমন সব ঘটনার ফল যেগুলো না ঘটলে তারা ঘটুক- এমন ইচ্ছা হতো। আমার মনে হয় ক্ষুধা তৃপ্তি যখন চলছে তখন তাকে গতীয় আনন্দ বলা যেতে পারে কিন্তু ক্ষুধা সম্পূর্ণ তৃপ্ত হওয়ার পর যে শান্তির অবস্থা আসে তাকে বলা যেতে পারে স্থিতীয় আনন্দ। এপিকুরসের মতে এই দুই প্রকারের ভিতরে দ্বিতীয়টি অনুসরণ করাই অধিক বিচক্ষণতা, কারণ, এটা নির্ভেজাল ও এক্ষেত্রে আকাক্ষার উত্তেজকরূপে বেদনার অস্তিত্ব প্রয়োজন হয় না। দেহ যখন ভারসাম্যের অবস্থায় থাকে তখন বেদনা থাকে না, সুতরাং ভারসাম্যের অবস্থা এবং অধিক উদ্দাম আনন্দের বদলে শান্ত আনন্দই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। মনে হয়, এপিকুরস চাইতেন সম্ভব হলে সবসময়ই মিতাহারী হয়ে থাকা এবং কখনোই ভোজনের অত্যধিক আকাক্ষা না থাকা।
সুতরাং কার্যক্ষেত্রে তিনি আনন্দের অস্তিত্বের চাইতে বেদনার অনস্তিত্বকেই জ্ঞানী ব্যক্তির লক্ষ্য মনে করতেন। একাধিক বস্তুর মূল থাকতে পারে পাকস্থলিতে কিন্তু পাকস্থলির বেদনার গুরুত্ব অতিভোজনের আনন্দের গুরুত্বের চাইতে অধিক, সেই জন্য এপিকুরস রুটি খেয়ে থাকতেন, শুধুমাত্র ভোজের দিন একটু পনীর খেতেন। সম্পদ ও সম্মানের আকাঙ্ক্ষা অর্থহীন, কারণ, এগুলো মানুষকে চঞ্চল করে অথচ সে সময় তিনি তৃপ্তিতে থাকতে পারতেন। বিচক্ষণতাই সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ : এটি মূল্যবান, এমনকি দর্শনশাস্ত্রের চেয়েও। তার বোধ অনুসারে দর্শনশাস্ত্র একটি ব্যবহারিক তন্ত্র, এটা তৈরি হয়েছে সুখী জীবন সৃষ্টি করার জন্য। এর জন্য প্রয়োজন শুধুমাত্র সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান, প্রয়োজন নেই যুক্তিবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র কিংবা প্লাতন নির্দেশিত বিধিমতো কোনো জটিল শিক্ষার। তিনি তাঁর তরুণ শিষ্য ও বন্ধু পুথক্লেস (Pythocles) কে জোরের সঙ্গে বলেছিলেন সমস্ত রকম সংস্কৃতি থেকে পালাও। তাঁর নীতিগুলোর স্বাভাবিক। পরিণতিতে তিনি জনজীবন থেকে দূরে থাকতে বলতেন, কারণ, মানুষের ক্ষমতা বাড়াবার অনুপাতে হিংসুকদের সংখ্যা বাড়বে, সুতরাং তারা তাকে আঘাত করার চেষ্টা করবে। এমনকি বাইরের দুর্ভাগ্যের হাত থেকে রক্ষা পেলেও ঐ পরিস্থিতিতে মানসিক শান্তি পাওয়া অসম্ভব হবে। জ্ঞানী মানুষ বাঁচতে চেষ্টা করবেন অলক্ষিত ভাবে যাতে তার কোনো শক্ত না হয়।
যৌনপ্রেম সর্বাধিক গতীয় আনন্দ হওয়ার ফলে সেটা স্বাভাবিকভাবেই বাধানিষেধের অন্তর্ভুক্ত। এই দার্শনিকের ঘোষণা যৌনসঙ্গম কখনো কোনো মানুষের ভালো করেনি এবং ক্ষতি কিছু না করে থাকলে তিনি ভাগ্যবান। তিনি শিশুদের (অন্যের শিশুদের) ভালোবাসতেন কিন্তু মনে হয় এই রুচির তৃপ্তির জন্য তিনি নির্ভর করতেন অন্যরা তাঁর উপদেশ অমান্য করবে এর উপর। আসলে মনে হয় তিনি তাঁর শ্রেয়তর বিচারবুদ্ধির বিরুদ্ধেই শিশুদের ভালোবাসতেন, কারণ, তাঁর মতে বিবাহ এবং সন্তান আরও গুরুত্বপূর্ণ কর্ম থেকে মানুষের মনকে বিক্ষিপ্ত করে। লুক্রেতিয়স, যিনি প্রেমের উপর দোষারোপ করার ব্যাপারে এপিকুরসকে অনুসরণ করতেন, তাঁর মতে ভাবাবেগ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে যৌনসঙ্গমে কোনো দোষ নেই।
এপিকুরসের মতে সবচেয়ে নিরাপদ সামাজিক আনন্দ হলো বন্ধুতা। বেন্থাম-এর মতো এপিকুরসও এমন একজন মানুষ ছিলেন যিনি মনে করতেন মানুষ সবসময়ই নিজের আনন্দ খুঁজে বেড়ায় কখনো বোকার মতো, কখনো জ্ঞানীর মতো কিন্তু বেন্থামেরই মতো তিনি নিজের সহে ও সদয় ব্যবহারের দ্বারা বিপথে চালিত হয়ে প্রশংসাযোগ্য আচরণ করতেন অথচ তাঁর তত্ত্ব অনুসারেই এরকম আচরণ থেকে বিরত থাকা উচিত ছিল। স্পষ্টতই তিনি বন্ধুদের পছন্দ করতেন তাদের কাছ থেকে কী পেলেন সে কথা না ভেবেই কিন্তু তাঁর দর্শন মানুষকে যেরকম স্বার্থপর মনে করে তিনি যে সেরকমই একথা নিজেকে বিশ্বাস করাতেন। কিকের-র তথ্য অনুসারে তার মত ছিল বন্ধুত আনন্দ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না এবং সে জন্যই এর চর্চা করতে হবে। কারণ, এছাড়া আমরা নিরাপদে ও নির্ভয়ে বাঁচতে পারি না, এমনকি আনন্দের সঙ্গেও নয়। কখনো কখনো তিনি তাঁর তত্ত্ব, কমবেশি ভুলে গিয়েছেন? তিনি বলছেন, সমস্ত বন্ধুত্বই স্বকীয়ভাবে আকাক্ষিত, যোগ করেছেন যদিও এটা শুরু হয় সাহায্যের প্রয়োজন থেকে।
এপিকুরসের নীতি অপরের কাছে পাশবিক এবং নৈতিক মহিমায় ন্যূন মনে হলেও তিনি অতিশয় আন্তরিক ছিলেন। যেমন আমরা দেখেছি তিনি বাগানে বসে গোষ্ঠীকে আমাদের পবিত্র দেহ বলেছেন। তাঁর লেখা একটি বইয়ের নাম পবিত্রতা সম্পর্কে (On Holiness), তার ভিতরে ধর্ম সংস্কারের সবরকম উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল মানুষের দুঃখদুর্দশা সম্পর্কে তার তীব্র করুণামণ্ডিত ভাবাবেগ অবশ্যই ছিল এবং অনমনীয় বিশ্বাস ছিল যে, মানুষ তাঁর দর্শন গ্রহণ করলে তাদের দুর্দশা অনেকাংশেই হ্রাস পাবে। এই দর্শন দুর্বলের দর্শন, এ দর্শন সৃষ্টি হয়েছিল এমন একটি বিশ্বের জন্য যে বিশ্বে দুঃসাহসী অভিযাত্রীর আনন্দ ছিল প্রায় অসম্ভব। স্বল্পাহার করো বদহজমের ভয়ে, স্বল্প পান করো খোয়ারির ভয়ে, রাজনীতি, প্রেম ও সমস্ত তীব্র ভাবাবেগ পরিহার কর, বিয়ে করে ও সন্তানের জনক-জননী হয়ে ভাগ্যের জামিন হয়ো না, মানসিক জীবনে নিজেকে শিক্ষা দাও বেদনার চেয়ে আনন্দের ধ্যান করতে। দৈহিক বেদনা নিশ্চয়ই অতীব মন্দ কিন্তু তীব্র হলেও তা ক্ষণস্থায়ী এবং দীর্ঘস্থায়ী হলেও মানসিক নিয়মানুবর্তিতায় তা সহনীয় হয় ও বেদনা সত্ত্বেও আনন্দের চিন্তার অভ্যাস দিয়ে সে বেদনা সহ্য করা যায়। সর্বোপরি, এমনভাবে বাঁচো যাতে ভয় এড়ানো যায়।
ভয়কে এড়ানোর সমস্যার মাধ্যমেই এপিকুরস তাত্ত্বিক দর্শনশাস্ত্রে প্রবেশ করেন। তাঁর মতে ভয়ের বৃহত্তম উৎস ধর্ম এবং মৃত্যুভয়, এগুলো পরস্পর সংযুক্ত, কারণ, মৃতরা অসুখী- এই দৃষ্টিভঙ্গিকে ধর্ম উৎসাহিত করে। সেইজন্য তিনি একটি অধিবিদ্যা অনুসন্ধান করলেন, যে বিদ্যা প্রমাণ করবে দেবতারা মানুষের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে এবং দেহের সঙ্গেই আত্মার মৃত্যু হয়। অধিকাংশ আধুনিক মানুষের ধারণা- ধর্ম হলো সান্ত্বনা কিন্তু এপিকুরসের কাছে ব্যাপারটা ছিল বিপরীত। প্রকৃতির ক্রিয়ায় অতিপ্রাকৃত হস্তক্ষেপ ছিল তাঁর কাছে একটা ভীতির উৎস এবং বেদনামুক্তির আশার পক্ষে অমরত্ব মারাত্মক। সেভাবে তিনি এক বিস্তৃত মতবাদ তৈরি করেছিলেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ভীতিসঞ্চারকারী বিশ্বাস থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়া।
এপিকুরস ছিলেন বস্তুবাদী কিন্তু নিয়তিবাদী নয়। বিশ্ব পরমাণু এবং শূন্যতা দিয়ে গঠিত- দেমক্রিতসের এই বিশ্বাসের তিনি অনুগামী ছিলেন কিন্তু দেমক্রিতসের মতো বিশ্বাস করতেন না যে, পরমানুগুলো সবসময় প্রাকৃতিক বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আমরা দেখেছি প্রাচীন গ্রিসের প্রয়োজনের কল্পনাকে বাঁচিয়ে রেখে ধর্মের বিরুদ্ধে আক্রমণ হবে অসম্পূর্ণ- এপিকুরসের এ বিচার হয়তো সঠিক ছিল। তার পরমাণুগুলোর ওজন ছিল। এবং সেগুলো ছিল অবিরাম পতনশীল- পৃথিবীর কেন্দ্র অভিমুখে নয় কিন্তু নিম্নগতি ছিল কোনো এক পরম অর্থে। কিন্তু যখন তখন একটি পরমাণু স্বাধীন ইচ্ছার মতো কোনো কিছুর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সরাসরি নিম্নগামী পথ থেকে সামান্য সরে যায়২৩ এবং তার ফলে অন্য কোনো পরমাণুর সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এই বিন্দু থেকে ঘূর্ণির সৃষ্টি ইত্যাদি দেমক্রিতস অনুসৃত পথে অগ্রসর হয়। আত্মা হলো বস্তু, শ্বাস ও তাপের মতো কণিকা দিয়ে গঠিত। (এপিকুরসের চিন্তনে শ্বাস ও বাতাস বায়ু থেকে পৃথক বস্তু, তারা শুধুমাত্র গতিশীল বায়ু নয়)। আত্মা পরমাণু সমগ্র দেহে বণ্টিত। অনুভূতির কারণ দেহগুলো থেকে পাতলা পর্দা পরিত্যক্ত হওয়া- আত্মা-পরমাণুগুলো স্পর্শ না করা পর্যন্ত তারা ভ্রাম্যমাণ থাকে। যে দেহগুলো থেকে তারা প্রথম চলতে শুরু করেছিল সেই দেহগুলো বিগঠিত হলেও পর্দাগুলোর অস্তিত্ব থাকতে পারে, এটাই স্বপ্নের কারণ। মৃত্যুতে আত্মা সর্বদিকে বিকীর্ণ হয়, তার পরমাণুগুলো অবশ্যই বেঁচে থাকে কিন্তু তাদের অনুভব করার ক্ষমতা থাকে না, কারণ, দেহের সঙ্গে তাদের সংযোগ তখন বিচ্ছিন্ন হয়। এপিকুরসের ভাষায়, এ থেকে বোঝা যায় আমাদের কাছে মৃত্যু কিছুই নয়, কারণ, যা বিগঠিত হয় তার কোনো অনুভূতি থাকে না এবং যার অনুভূতি থাকে না তার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।
দেবতাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে এপিকুরসের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যেহেতু দেবতা সম্পর্কে কল্পনের ব্যাপক অস্তিত্বের এছাড়া অন্য কোনো কারণ তিনি দেখতে পারেননি। তবে তাঁর প্রতীতি জন্মেছিল মানবিক জগতের ব্যাপার নিয়ে দেবতারা মাথা ঘামান না। তাঁরা বুদ্ধিমান ভোগবাদী, এপিকুরসের নীতি তারা মেনে চলেন এবং জনজীবন থেকে সরে থাকেন, তাঁদের কাছে শাসনকার্য একটি অপ্রয়োজনীয় শ্রম, তাঁদের পূর্ণ প্রশান্তির জীবনে এ কর্মের প্রতি কোনো আকর্ষণ তাঁরা অনুভব করেন না। অবশ্যই ভবিষ্যদ্বাণী করা, ভাগ্য গণনা ও এই জাতীয় কাজকর্ম করা নিখাদ কুসংস্কার ছাড়া কিছু নয় এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপর বিশ্বাসও সে ধর্মের কুসংস্কার।
সুতরাং, দেবতাদের ক্রোধের পাত্র হতে পারি কিংবা মৃত্যুর পর হাদেস (Hades) এ কষ্ট পেতে পারি এরকম ভয়ের কোনো ভিত্তি নেই। প্রকৃতির বলগুলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পাঠযোগ্য, আমরা সেই বলগুলোর অধীন হলেও আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা আছে এবং কিছু পরিমাণে আমরা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্যবিধাতা। মৃত্যুকে আমরা এড়াতে পারি না কিন্তু সঠিকভাবে বুঝলে মৃত্যু মন্দ কিছু নয়। এপিকুরসের নীতি মেনে বিচক্ষণভাবে জীবনযাপন করলে হয়তো আমরা বেদনা থেকে খানিকটা মুক্তি পাব। এটা একটা সংযমের আপ্তবাক্য কিন্তু মানবিক দুঃখে গভীরভাবে অভিভূত মানুষের মনে উদ্দীপনা সৃষ্টির পক্ষে এই আপ্তবাক্য যথেষ্ট।
বিজ্ঞানের জন্যই বিজ্ঞানের প্রতি কোনো আকর্ষণ এপিকুরসের নেই, যে সব পরিঘটনাগুলোকে কুসংস্কারের কারণে ভগবানের গুণ বলে মনে হয় সেগুলোর প্রকৃতিভিত্তিক ব্যাখ্যা দানের জন্য তাঁর কাছে বিজ্ঞানের মূল্য আছে। যখন প্রকৃতিগত একাধিক ব্যাখ্যা রয়েছে, এপিকুরসের মতে, তখন তার ভিতরে কোনটা সঠিক সেটা বেছে নেওয়ার চেষ্টার কোনো অর্থ হয় না। উদাহরণ, চাঁদের দশার নানারকম ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ না দেবতাদের টেনে আনা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত একটার সঙ্গে আর একটার কোনো পার্থক্য নেই এবং সেগুলোর ভিতরে কোনটা সঠিক সেটা নির্ধারণ করার চেষ্টা অলস কৌতূহল মাত্র। এপিকুরীয়দের যে প্রাকৃতিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোনো অবদান নেই সেটা বিস্ময়কর নয়। পরবর্তী পৌত্তলিকদের জাদুবিদ্যা, জ্যোতিষ এবং ভবিষ্যদ্বাণীতে বর্ধমান বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদরূপে এই মতগুলো একটি প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সাধন করেছিল কিন্তু তাঁদের প্রতিষ্ঠাতার মতোই সেই মতগুলো ছিল গোঁড়া, সীমাবদ্ধ এবং ব্যক্তিগত সুখ ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে অকৃত্রিম আকর্ষণহীন। তাঁরা এপিকুরসের মতগুলো মুখস্থ করতেন। কিন্তু তাঁদের গোষ্ঠীর কয়েক শতাব্দীব্যাপী জীবনকালের ভিতরে নতুন কিছু যোগ করেননি।
এপিকুরসের একমাত্র বিখ্যাত শিষ্য কবি লুক্ৰেতিয়স (Lucretius) ছিলেন জুলিয়স সীজারের সমসাময়িক (তাঁর জীবনকাল ৯৯-৫৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ)। রোমক গণতন্ত্রের শেষদিকে স্বাধীন চিন্তাই ছিল। ফ্যাশন এবং এপিকুরসের মতবাদ শিক্ষিতদের ভিতরে জনপ্রিয় ছিল, সম্রাট অগস্তস (Augustus) প্রাচীন সদগুণ এবং প্রাচীন ধর্মের পুরোনো ধরনে পুনর্জীবন ঘটান, তার ফলে লুক্রেতিয়সের বস্তুগুলোর প্রকৃতি সম্পর্কে (On the Nature of Things) কবিতাটি জনপ্রিয়তা হারায় এবং রেনেসাঁ না হওয়া পর্যন্ত সেরকমই থেকে যায়। মধ্যযুগের পর কবিতাটির একটিমাত্র পাণ্ডুলিপির অস্তিত্ব ছিল এবং সেটিও গোঁড়াদের ধ্বংসকার্য থেকে অল্পের জন্য বেঁচে যায়। কোনো বড় কবিকে স্বীকৃতির জন্য কদাচিৎ এত দীর্ঘ প্রতীক্ষা করতে হয়েছে কিন্তু আধুনিক যুগে তাঁর প্রতিভা প্রায় সকলের কাছে স্বীকৃতি লাভ করেছে। উদাহরণ, তিনি এবং বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ছিলেন শেলীর প্রিয় লেখক।
তাঁর কবিতা এপিকুরসের দর্শনকে কাব্যে প্রকাশ করেছে। যদিও দুজনের মতবাদ অভিন্ন, তাঁদের মেজাজে ছিল অনেক পার্থক্য। লুক্রেতিয়সের ছিল তীব্র ভাবাবেগ এবং এপিকুরসের তুলনায় তার উৎসাহের প্রয়োজন বেশি ছিল বিচক্ষণতার চেয়ে। তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন এবং মনে হয়, মাঝে মাঝে উন্মাদরোগে আক্রান্ত হতেন- কেউ কেউ নিশ্চিতভাবে ঘোষণা করেন এ রোগের কারণ ছিল প্রেমের বেদনা অথবা কামোদ্দীপক ভেষজের অনভিপ্রেত ক্রিয়া। একজন ত্রাতার প্রতি যে মনোভাব, এপিকুরসের প্রতি তাঁর সেই মনোভাব এবং যে মানুষকে তিনি ধর্মের ধ্বংসকারী মনে করতেন তাঁর সম্পর্কে তিনি প্রয়োগ করেছেন ধর্মীয় তীব্রতাবোধক ভাষাঃ
যখন আনত মানবজীবন ছিল ভূমিতে শায়িত
ছিল পদতলে দলিত এবং অন্যায়ভাবে মথিত
ধর্মের নিষ্ঠুরতার নিচে, সেইসময়
উপরে গগনলোক থেকে।
দেখা দিল স্ত্রীমুখ, সে আনত ছিল মর-মানুষের দিকে।
ভয়ংকর তার অবয়ব, গ্রিসের এক মানুষ প্রথম
সাহস পেলেন তার বিরুদ্ধে নিজের মন-চোখ খুলতে
তিনি প্রথম উঠে দাঁড়িয়েছিলেন আর (আহবান করেছিলেন দ্বন্দে)।
তাঁকে শান্ত করতে পারেনি দেবতাদের কল্প কাহিনি কিংবা বজ্রবিদ্যুৎ
কিংবা আকাশ থেকে গুড়গুঁড়িয়ে ভয় দেখানো,
বরং তারা উদ্বুদ্ধ করেছে তার আত্মার বীর্যকে,
তাঁর সাহসকে, তখনও তার আকাঙ্ক্ষা তিনিই প্রথম
ভেঙে ফেলবেন, খুলে দেবেন প্রকৃতির কঠিনভাবে রুদ্ধ দুয়ার।
তাই তো জিতে গেল তার মানসিক তেজ, এবং
তাই তো তিনি এগিয়ে গেলেন! এগিয়ে গেলেন
বিশ্বের প্রজ্জ্বলিত বেষ্টনী ছাড়িয়ে,
চিত্তে আর মনে দূর প্রসারিত হলো গতি এবং
সে গতি অপরিমাপিত সম্পূর্ণ মহাবিশ্বে, তারপর
তিনি বিজয়ী হয়ে ফিরে আসেন, সঙ্গে নিয়ে আসেন।
জ্ঞান, সে জ্ঞান, কি অস্তিমান হতে পারে আর কি পারে না
অস্তিমান হতে তার, আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন সূক্ষ্মভাবে
সে শিক্ষা প্রতিটি বস্তুর তত্ত্বের শক্তি
কিসের উপর নির্ভর করে তার সীমা আর তার
গভীরে প্রোথিত বেষ্টনীর প্রস্তুরসীমা।
সুতরাং ধর্মকে এখন পরিত্যাগ করা হয়েছে।
তারা পিষ্ট হয়েছে মানুষের পদতলে এবং পালা করে
পদপিষ্ট হয়েছে? আমরা আকাশের মতো উঁচু হয়ে
অভিনন্দন জানাই ভঁর বিজয়কে।
যদি গ্রিক ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রফুল্ল সম্পর্কিত প্রথাগত বিবরণ কেউ মেনে নেন তাহলে এপিকুরস ও লুক্ৰেতিয়সের প্রদর্শিত ধর্মের প্রতি ঘৃণাকে বোঝা খুব সহজ নয়। উদাহরণ- কীটসের গ্রিক ঘট সম্পর্কে গীতিকবিতা (Ode on a Grecian Urn) একটি ধর্মীয় উত্সব উদযাপন করা সম্পর্কে কিন্তু সে উৎসব এমন নয় যা মানুষের মনকে অন্ধকারময় ও বিষণ্ণ ভীতিতে পূর্ণ করতে পারে। আমার মনে হয় সাধারণ লোকের বিশ্বাস এরকম আনন্দপ্রধান ছিল না। গ্রিক ধর্মের অন্য অবয়বের তুলনায় অলিম্পীয়দের পূজায় কুসংস্কার জনিত নিষ্ঠুরতা কম ছিল কিন্তু খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত, এমনকি অলিম্পীয় দেবতারাও মাঝে মাঝে নরবলি দাবি করেছেন এবং এই রীতি পুরাণে ও নাটকে নথিভুক্ত আছে। সমগ্র বর্বর জগতে এপিকুরসের কাল পর্যন্ত নরবলি স্বীকৃত ছিল। রোমকদের বিজয়কালের পূর্বে, পিউনিক যুদ্ধের মতো সঙ্কটকালে, এমনকি বর্বরদের ভিতরেও যারা সভ্যতম- তারা এ রীতি মানত।
জেন হ্যারিসন (Jane Harrison) সবচাইতে বিশ্বাসযোগ্যভাবে দেখিয়েছেন জিউস ও তাঁর পরিবারের পূজা ছিল গ্রিকদের সরকারি ধর্ম, এছাড়াও তাদের অনেক আদিম বিশ্বাস ছিল ও তার সঙ্গে জড়িত ছিল কমবেশি অনেক বর্বর আচার-অনুষ্ঠান। এর খানিকটা মিশে গিয়েছিল অরফীয়বাদের সঙ্গে, ধর্মীয় মানসিকতার মানুষদের ভিতরে এটা ছিল প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস। অনেক সময় অনুমান করা হয় নরক একটি খ্রিষ্টিয় আবিষ্কার কিন্তু এ চিন্তন ভুল। এ বিষয়ে খ্রিষ্টধর্ম যা করেছিল তা হলো শুধুমাত্র আদিকালের প্রচলিত বিশ্বাসকে সুসংবদ্ধ করা। প্লাতনের রিপাবলিকের শুরু থেকে একথা স্পষ্ট যে, মৃত্যুর পর শাস্তির ভয় পঞ্চম শতাব্দীর আথিনাতে বেশ ব্যাপক ছিল এবং সক্রাতেস ও এপিকুরসের মধ্যবর্তী সময়ে সে ভয় যে কমেছিল এরকম মনে হয় না। (আমি শিক্ষিত সংখ্যালঘুদের কথা ভাবছি না কিন্তু ভাবছি সাধারণ মানুষের কথা)। তাছাড়া, নিশ্চিতভাবে প্লেগ, ভূমিকম্প, যুদ্ধে পরাজয় এবং এই জাতীয় বিপর্যয়কে ঐশ্বরিক অসন্তোষ বলে ভাবা কিংবা অশুভ লক্ষণকে অমান্য করার মতো ভুলের উপর আরোপ করার অভ্যাস ব্যাপক ছিল। আমার মনে হয় সাধারণের বিশ্বাস সম্পর্কে গ্রিক সাহিত্য শিল্প সম্ভবত ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করে। যদি অভিজাতদের বই ও অঙ্কিত চিত্রাবলি ছাড়া অন্য সবকিছুই দুষ্প্রাপ্য হতো তাহলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিককার মেথডিজম (Methodism-ইংল্যান্ডের কঠোর নিয়মনিষ্ঠ খ্রিষ্টিয় সম্প্রদায় বিশেষের আচরণ ও মতবাদ-অনুবাদক) সম্পর্কে আমরা কী জানতে পারতাম? হেলেনায়িত যুগে ধার্মিকতার মতো মেথডিজমের প্রভাবের উত্থান হয়েছিল নিচু থেকে। বসওয়েল (Boswell) ও স্যার জোসুয়া রেনল্ডস, (Sir Joshua Reynolds)-দের আগে থেকেই মেথডিজম ক্ষমতাশালী ছিল, যদিও তাঁদের পরোক্ষ উল্লেখ থেকে এই প্রভাবের শক্তি বোঝা যায় না। সেইজন্য গ্রিক ঘট (Grecian Urn)-এর উপরকার চিত্র দেখে কিংবা কবি ও অভিজাত দার্শনিকদের লেখা থেকে আমাদের কখনোই গ্রিক জনসাধারণের ধর্ম বিচার করা উচিত নয়। এপিকুরস জন্মসূত্রে কিংবা তাঁর সহযোগীদের মাধ্যমে অভিজাত ছিলেন না, হয়তো এই তথ্যই ধর্মের সঙ্গে তার অসাধারণ শত্রুতার ব্যাখ্যা।
রেনেসাঁ-র পর প্রধানত লুক্রেতিয়সের কবিতার মাধ্যমে এপিকুরসের দর্শন পাঠকদের কাছে পরিচিত হয়। তারা যদি পেশাদার দার্শনিক না হয়ে থাকেন তাহলে তাঁদের সর্বাপেক্ষা চমৎকৃত করেছে বস্তুবাদ, বিধাতার অনুগ্রহকে অস্বীকার এবং অমরত্বের কল্পনকে বর্জন ইত্যাদি এপিকুরীয় দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে খ্রিষ্টিয় বিশ্বাসের বৈপরীত্য। আধুনিক পাঠকদের বিশেষভাবে নাড়া দেয় এইসমস্ত দৃষ্টিভঙ্গি (আজকাল এগুলোকে মনে হয় হতাশ এবং বিষণ্ণ চিন্তন), এগুলোকে উপস্থাপিত করা হয়েছিল ভয়ের বোঝা থেকে মুক্তিলাভের সহায়ক শাস্ত্রীয় বচনরূপে। লুক্ৰেতিয়স ধর্মের ব্যাপারে সত্য বিশ্বাস সম্পর্কে যে কোনো খ্রিষ্টানের মতোই কঠিন বিশ্বাসী। অন্তর্দ্বন্দ্বের বলি হয়ে মানুষ যখন নিজের কাছ থেকে পালাতে চায় তখন তারা নিষ্ফলভাবে স্থান পরিবর্তনের সাহায্যে মুক্তি খোঁজে, এইসবের বিবরণ দিয়ে লুক্রেতিয়স বলছেনঃ
প্রতিটি মানুষ পলায়ন করে নিজের কাছ থেকে,
তবুও বস্তুত নিজের কাছ থেকে পালানোর কোনো
ক্ষমতা তার নেই : নিজের বিদ্বেষেই সে তাকে জড়িয়ে ধরে,
আবার ঘৃণাও করে তাকে, কারণ সে নিজে অসুস্থ হলেও
তার রোগের কারণ সে বোঝে না।
সেটা যদি বুঝতে পারত সঠিকভাবে, তাহলে সবাই,
অন্যসব কাজ ত্যাগ করে প্রথমে চেষ্টা করত,
বিশ্বের প্রকৃতি বুঝতে শিখতে,
যেহেতু অনন্তকালের ভিতরে এটাই আমাদের অবস্থা,
শুধুমাত্র যাতে আমাদের সন্দেহ, সেই একঘণ্টার জন্যই নয়,
যার ভিতর দিয়ে যেতে হবে, সমস্ত মর-জীবকেই
যেতে হবে সমকাল জুড়ে, সে কাল অপেক্ষা করে,
তাদের জন্য মৃত্যুর পর।
এপিকুরসের যুগ ছিল ক্লন্তির যুগ এবং আত্মার কঠোর পরিশ্রমের তুলনায় নির্বাণকে মনে হতে পারত স্বাগত বিশ্রাম। এর বিপরীতে, গণতন্ত্রের শেষ যুগ অধিকাংশ রোমকদের কাছে মোহমুক্তির যুগ ছিল না : বিশাল কর্মশক্তি সম্পন্ন মানুষেরা চরম। বিশৃঙ্খলা থেকে নতুন শৃঙ্খলা সৃষ্টি করছিল, মাকেদনীয়রা এ কাজ করতে অক্ষম হয়েছিল। কিন্তু যেসব রোমক অভিজাতরা রাজনীতি থেকে দূরে থাকতেন এবং ক্ষমতা ও লুণ্ঠনের দ্বন্দ্ব নিয়ে মাথা ঘামাতেন না, তাঁদের কাছে ঘটনাবলি নিশ্চয়ই গভীর নিরাশাব্যঞ্জক ছিল। এর সঙ্গে পৌনঃপুনিক পাগলামি যদি যুক্ত হয় তবে লুক্রেতিয়সের পক্ষে নির্বাণের আশাকে মুক্তি বলে গ্রহণ করার মধ্যে আশ্চর্যের কিছু নেই।
কিন্তু মৃত্যুভয় সহজাত প্রবৃত্তিতে এমন গভীরভাবে প্রোথিত যে, এপিকুরসের শাস্ত্র জনসাধারণের ভিতর কোনোকালেই আবেদন রাখতে পারেনি। এটা সবসময়ই রয়ে গিয়েছিল এক সংখ্যালঘু সুসংস্কৃত সম্প্রদায়ের ধর্ম। আগস্তসের সময়ের পর থেকে, এমনকি দার্শনিকদের মধ্যেও এই দর্শন বর্জন করে স্টোইকবাদকে গ্রহণ করা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ কথা সত্যি-এই দর্শন এপিকুরসের মৃত্যুর পর ছশ বছর পর্যন্ত ক্ষীয়মাণ প্রাণশক্তি নিয়েও বেঁচেছিল। কিন্তু পার্থিব অস্তিত্বের দুঃখে বর্ধমানভাবে ভারাক্রান্ত মানুষ দর্শন কিংবা ধর্মের কাছ থেকে অবিচ্ছিন্নভাবে আরও শক্তিশালী ওষুধ দাবি করতে লাগল। কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদে দার্শনিকরা আশ্রয় নিলেন নবপ্নাতনবাদে, অশিক্ষিতরা আশ্রয় নিলেন পূর্বদেশীয় নানারকম কুসংস্কারে এবং তারপর নিরবচ্ছিন্ন বর্ধমান হারে খ্রিষ্টধর্মে। এই ধর্ম তার আদি অবয়বে সমস্ত উত্তমকেই স্থাপন করেছিল মৃত্যুর পরবর্তী সময়ে, এইভাবে তারা মানুষকে এমন একটি ধর্মশাস্ত্র দান করলেন যা এপিকুরসদত্ত শাস্ত্রের (gospel) ঠিক বিপরীত। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এপিকুরসের ধরনের মতবাদগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন আলোকপ্রাপ্ত ফরাসি দার্শনিকরা এবং বেন্থাম ও তাঁর অনুগামীরা একে ইংল্যান্ডে নিয়ে এসেছিলেন। এটা করা হয়েছিল খ্রিষ্টধর্মের সচেতন বিরোধিতা করতে, এপিকুরস তদানীন্তন ধর্মের যেমন বিরোধী ছিলেন খ্রিষ্টধর্ম সম্পর্কে এরাও ছিলেন সেরকম।