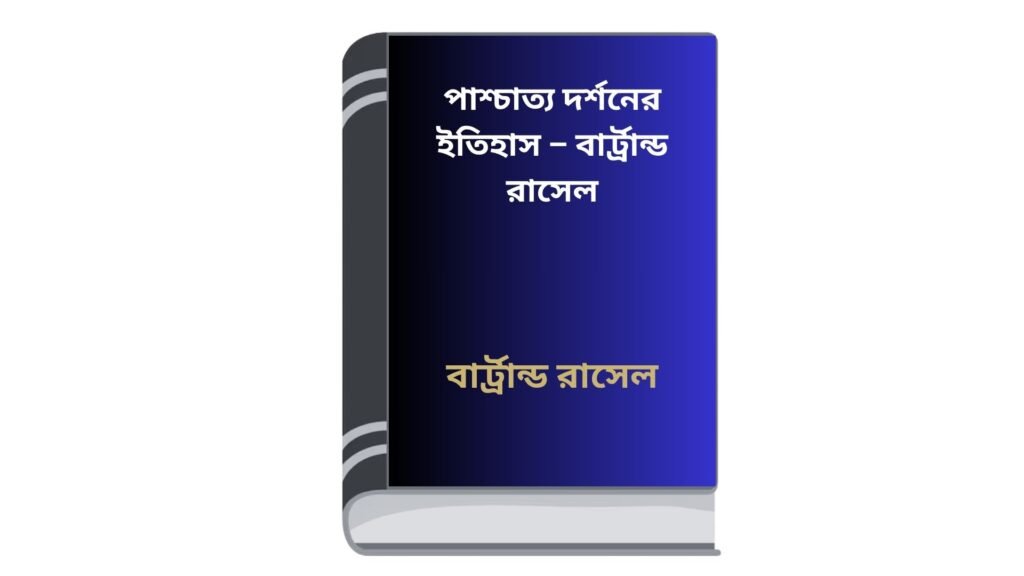০৪. হেরাক্লিডস
৪. হেরাক্লিডস
গ্রিকদের সম্পর্কে বর্তমানকালে সাধারণত দুটি বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়। প্রথমত-রেনেসাঁ (নবজাগরণ) থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত গ্রিকদের সম্পর্কে প্রায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভক্তি, গ্রিকদের প্রতি এই ভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ সবকিছুর আবিষ্কর্তা হিসেবে এবং আধুনিক মানুষের পক্ষে অতিমানবিক ক্ষমতাশালী সেই গ্রিকদের সমকক্ষ হওয়া অসম্ভব। দ্বিতীয়ত-বিজ্ঞানের জয় এবং প্রগতি সম্পর্কে আশাবাদী বিশ্বাস দ্বারা অনুপ্রাণিত। তাঁদের ধারণা প্রাচীনদের কর্তৃত্ব এক দমবন্ধ করা দুঃস্বপ্ন এবং চিন্তা জগতে তাদের দানের বেশির ভাগ এখন ভুলে যাওয়াই শ্রেয়। আমি নিজে এই দুটি চরম দৃষ্টিভঙ্গির একটিও গ্রহণ করতে অক্ষম; আমার বক্তব্য-দুটি মতই অংশত সত্য, অংশত নয়। বিস্তৃত আলোচনার আগে আমি বলতে চেষ্টা করব গ্রিক চিন্তাধারা পাঠ করে কী ধরনের প্রজ্ঞা আমরা আজও লাভ করতে পারি।
বিশ্বের প্রকৃতি এবং গঠন সম্পর্কে নানা প্রকল্প সম্ভব। যতদিন অধিবিদ্যার অস্তিত্ব ছিল ততদিন অধিবিদ্যার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত প্রকল্প ক্রমশ সংস্কৃত হয়েছে, তাদের নিহিতার্থ বিকশিত হয়েছে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রকল্পের সমর্থকদের আপত্তির ফলে প্রতিটি পুনর্গঠিত হয়েছে। প্রতিটি তন্ত্র অনুসারে ব্রহ্মাণ্ড বিষয়ক চিন্তন এক পরমানন্দদায়ক কল্পনা এবং গোঁড়ামির প্রতিষেধক। তাছাড়া যদি কোনো প্রকল্পের প্রদর্শন করা না যায়, তাহলেও জানিত তথ্যের সঙ্গে প্রতিটিকে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য সেগুলোতে কী অক্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা আবিষ্কার করলে অকৃত্রিম জ্ঞান লাভ হয়। আধুনিক দর্শনের সবগুলো প্রকল্পের প্রথম চিন্তক গ্রিকরা; বিমূর্ত ব্যাপারে তাদের কল্পনার প্রসার এবং তজ্জনিত উদ্ভাবন ক্ষমতার উচ্চ প্রশংসার আধিক্য বোধ হয় সম্ভব নয়। গ্রিকদের সম্পর্কে আমার যা বক্তব্য তা প্রধানত এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। আমি মনে করি তারা এমন সব তত্ত্বের জন্মদান করেছেন যে তত্ত্বের নিজস্ব স্বাধীন জীবন ও বিকাশ ছিল এবং আছে। তত্ত্বগুলো প্রথমদিকে একটু অর্বাচীন হলেও সেগুলো দুহাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে টিকে থাকার এবং বিকাশ লাভ করার যোগ্যতা প্রমাণ করেছে।
এটা সত্য যে, গ্রিকরা বিমূর্ত চিন্তায় অন্য এমন কিছু দান করেছেন যার স্থায়ী মূল্য প্রমাণিত: তাঁরা গণিত আবিষ্কার করেছেন এবং আবিষ্কার করেছেন অবরোহী যুক্তি, বিশেষ করে, জ্যামিতি একটি গ্রিক আবিষ্কার-আধুনিক বিজ্ঞান সম্ভব হতো না যদি না জ্যামিতি থাকত। কিন্তু গণিতের সূত্রেই গ্রিক প্রতিভার একদেশদর্শিতা প্রকাশিত হয়: যা স্বপ্রকাশ মনে হয়েছে তার ভিত্তিতে তারা অবরোহী যুক্তি প্রয়োগ করেছেন, কিন্তু পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে আরোহী যুক্তি প্রয়োগ করেননি। এই পদ্ধতি প্রয়োগে তাদের আশ্চর্যজনক সাফল্যগুলো শুধুমাত্র আদিম বিশ্বকে বিপদগামী করেছে তাই নয়, বিপদগামী করেছে আধুনিক বিশ্বের অধিকাংশকে। ঘটনাগুলো পর্যবেক্ষণ করে আরোহী পদ্ধতিতে নীতি নির্ধারণ করার যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তা অতি ধীরে দার্শনিকদের মনগড়া ঝকঝকে স্বতঃসিদ্ধের ভিত্তিতে অবরোহী যুক্তি প্রয়োগের হেলেনীয় পদ্ধতিকে প্রতিস্থাপন করেছে। অন্য যুক্তি ছাড়াও এই জন্য গ্রিকদের সম্পর্কে প্রশ্নাতীত শ্রদ্ধা থাকা ভুল। কয়েকজনের ভিতরে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আভাস দেখতে পাওয়া যায় এবং তারাই প্রথম এ পদ্ধতির আভাস পেয়েছিলেন কিন্তু সাধারণভাবে এই পদ্ধতি গ্রিকদের মেজাজে অপরিচিত ছিল। সেই জন্য গত চারশ বছরের বৌদ্ধিক প্রগতিকে ছোট করে গ্রিকদের গৌরব করলে আধুনিক চিন্তা খর্বিত হয়।
পূজার মনোভাবের বিরুদ্ধে গ্রিক সাপেক্ষ কিংবা অন্য যে কারুর প্রতি একটি সাধারণ যুক্তিও রয়েছে। একজন দার্শনিকের দর্শন পাঠ করতে হলে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি-পূজা অথবা ঘৃণা নয়, প্রথমে থাকা উচিত কল্পনামূলক সমবেদনা। এই তত্ত্ব বিশ্বাস করলে কীরকম লাগে সেটা বোধগম্য হওয়া পর্যন্ত এই সমবেদনা থাকা উচিত। শুধুমাত্র তার পরেই সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি পুনরুজ্জীবিত হওয়া উচিত। যথাসম্ভব এই মনোভাব হওয়া উচিত জীবনব্যাপী দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করার মতো। ঘৃণাতে এই পদ্ধতির প্রথম অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পূজাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দ্বিতীয় অংশ। দুটি জিনিস স্মরণ রাখা উচিত: যার মতামত এবং তত্ত্ব পাঠযোগ্য তিনি ধীমান ছিলেন-এটা অনুমেয়, কিন্তু কেউই কোনো বিষয়ে সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত সত্যে পৌঁছেছেন-এরকম কোনো সম্ভাবনা নেই। কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি স্পষ্টতই অসম্ভব কোনো মত প্রকাশ করেন তাহলে সে মতকে যেনতেন প্রকারের সত্য প্রমাণ করার চেষ্টা করা উচিত। বরং উচিত সে মতটা কেন সত্য মনে হয়েছিল তার কারণ খুঁজে বার করা। ঐতিহাসিক আর মনস্তাত্ত্বিক কল্পনের এই প্রচেষ্টা তৎক্ষণাৎ আমাদের চিন্তার পরিধি পরিবর্তন করে এবং আমাদের সযত্নে রক্ষিত সংস্কারগুলো ভিন্নযুগের মানসিকতায় কতটা মূর্খতা মনে হতে পারে সেটা বুঝতে সাহায্য করে।
এই অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য হেরাক্লিস। তাঁর এবং পীথাগরাসের মধ্যবর্তী ক্সেনোফানেস (Xenophanes) নামে আর একজন দার্শনিক ছিলেন, তুলনায় তার গুরুত্ব কম। তাঁর কাল অনিশ্চিত, তিনি উল্লেখ করেছেন পীথাগরসকে এবং হেরাক্লিডস তাঁকে উল্লেখ করেছেন-প্রধানত এই দুটি তথ্যের ভিত্তিতে তাঁর কাল নির্ণয় করা হয়। যদিও জন্মসূত্রে ইওনীয়বাসী কিন্তু বেশির ভাগ সময় তিনি কাটিয়েছেন দক্ষিণ ইতালিতে। তাঁর বিশ্বাস ছিল সকল বস্তুই ক্ষিতি এবং জল থেকে সৃষ্ট। দেবতা বিষয়ে তার স্বাধীন চিন্তা ছিল খুব দৃঢ়। হোমের এবং হেসিয়দ (Hesiod) দেবতাদের উপর এমন সব বস্তু আরোপ করেছেন যা মরণশীলদের পক্ষে লজ্জার এবং নিন্দনীয়, যথা চৌর্য, ব্যভিচার এবং পরস্পরকে প্রতরণা-মরণশীলরা ভাবে তাদের মতোই দেবতাদেরও জন্ম হয়, পরিধেয় তাদের মতো-স্বর এবং আকারও…….হ্যাঁ, যদি ষাড়, ঘোড়া কিংবা সিংহদের হাত থাকত এবং তারা হাত দিয়ে আঁকতে পারত ও মানুষের মতো শিল্পকর্ম করতে পারত, তাহলে ঘোড়ারা দেবতাদের ছবি আঁকত ঘোড়ার আকৃতিতেই, ষাঁড় আঁকত ষাঁড়ের মতো এবং তাদের দেহ আঁকত নানাভাবে নিজেদের মতো করে। ইথিওপীয়রা তাদের দেবতা নির্মাণ করেন খ্যাদা নাক এবং কালো চেহারার। থ্রাকীয়রা বলেন তাঁদের বেদতার চোখ নীল এবং চুল লাল। তিনি এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন এবং বিশ্বাস করতেন তার আকার এবং চিন্তা মানুষের চাইতে অন্যরকম, তিনি বিনা পরিশ্রমে, শুধু মনের জোরে সবকিছুকেই নাড়া দেন। ক্সেনোফানেস পুথাগোরীয় পুনর্জন্মবাদ নিয়ে রসিকতা করতেন।
কথিত আছে, একবার তাঁর (পীথাগোরাসের) চলার পথে একটি কুকুরের উপরে যখন নির্দয় ব্যবহার করা হচ্ছিল তখন তিনি বলেছিলেন, থামো, ওকে মেরো না! একজন বন্ধুর আত্মা ওর ভিতরে রয়েছে! ওর গলার স্বর শুনে আমি বুঝতে পেরেছি। তাঁর বিশ্বাস ছিল ধর্মতত্ত্বের ব্যাপারে সত্য নির্ণয় করা অসম্ভব। দেবতা এবং যে সমস্ত বিষয় সম্পর্কে আমি বলছি সে বিষয়ে নিশ্চত সত্য সকলেরই অজানা, কেউ জানবেও না। হ্যাঁ, কেউ যদি ঘটনাচক্রে সম্পূর্ণ সত্যি কোনো কথা বলে ফেলে তাহলে সে নিজেও সেটা জানে না-অনুমান ছাড়া কোথাও কিছু নেই।
পীথাগোরাস এবং অন্যান্যদের রহস্যবাদী ঝোঁকের বিরোধী যুক্তিবাদীদের পরম্পরার ভিতরে ক্সেনোফানেসের স্থান রয়েছে কিন্তু স্বাধীন চিন্তক হিসেবে তিনি প্রথম শ্রেণির নন।
আমরা দেখেছি পীথাগোরাসের মতবাদ থেকে তাঁর শিষ্যদের মতবাদ পৃথক করা খুবই কঠিন, পুথাগরস নিজে যদিও খুবই প্রাচীন ছিলেন তবুও তাঁর মতবাদের প্রভাব পড়েছিল কিন্তু অন্যান্য বহু দার্শনিকের পরবর্তীকালে। এখনও পর্যন্ত প্রভাবশালী, এমন একটা তত্ত্ব আবিষ্কারকদের ভিতরে হেরাক্লিতসই প্রথম। তার কাল ৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি। তিনি এফেসাসের একজন অভিজাত নাগরিক ছিলেন-এছাড়া তাঁর জীবন সম্বন্ধে সামান্যই জানা যায়। সবকিছুই নিরন্তর পরিবর্তনশীল (ক্ষণিকবাদ)-প্রাচীনকালে এই মতবাদের জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন, কিন্তু দেখতে পাব এটা তার অধিবিদ্যার একটা দিক মাত্র।
হেরাক্লিডস ইওনীয়বাসী হলেও মিলেশীয়দের বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্য বহন করতেন না। তিনি রহস্যবাদী তবে একটু অদ্ভুত ধরনের। তিনি মনে করতেন, অগ্নি মূলগত বস্তু। প্রতিটি বস্তু আগুনের শিখার মতো অন্য কিছুর মৃত্যু থেকে জন্মগ্রহণ করে। মরণশীলরা অমর এবং অমররা মরণশীল-একজনের মৃত্যু থেকে আর একজনের জীবন ও আর একজনের জীবন থেকে অন্যজনের মৃত্যু। বিশ্বে ঐক্য রয়েছে কিন্তু এ ঐক্য বৈপরীত্যের সমন্বয়ে গঠিত। এক থেকে সব জিনিসের সৃষ্টি এবং সব জিনিস থেকে এক এর সৃষ্টি কিন্তু এক-এর চাইতে বহু-র বাস্তবতা কম-এক হলের ঈশ্বর।
তাঁর যে সমস্ত লেখা এখনও পাওয়া যায় তা থেকে মনে হয় তিনি অমায়িক মানুষ ছিলেন না। ঘৃণায় তাঁর আসক্তি ছিল এবং তিনি ছিলেন গণতন্ত্রের ঠিক বিপরীত। সহ নাগরিকদের সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যঃ প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক এফেসীয়দের গলায় দড়ি দেওয়াই ভালো এবং অজাতশত্রুদের হাতে নগরটা তুলে দেওয়া উচিত, কারণ, তাঁদের শ্রেষ্ঠ মানুষ হের্মোদরস (Hermodorus)-কে তাঁরা পরিত্যাগ করেছেন এই বলে, আমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কাউকে আমরা চাই না, এরকম কেউ থাকলে সে অন্য কোনোখানে থাক, অন্য লোকের ভিতরে সর্বশ্রেষ্ঠ হোক। একটি ব্যতিক্রম ছাড়া তিনি সমস্ত পূর্বসূরিদের নিন্দা করতেন। হোমেরকে তালিকা থেকে বার করে দিয়ে চাবকানো উচিত। এ পর্যন্ত যত লোকের আলোচনা আমি শুনেছি তাদের ভিতরে এমন একজনও নেই যিনি বুঝতে পারেন প্রজ্ঞা অন্য সব জিনিসের চাইতে পৃথক। বহু জিনিস শিখলেই বোঝা হয় না, এ না হলে হেসিয়দ এবং পীথাগোরাস বুঝতে শিখতেন, তাছাড়া বুঝতে শিখতেন ক্সেনোফানেস এবং হেকাতায়েয়স (Hecataeus)। পীথাগোরাস… যা তাঁর প্রজ্ঞা বলে দাবি করেছেন তা আসলে বহু জিনিস সম্পর্কে জ্ঞান এবং দুষ্টুমি। তাঁর নিন্দার একটি ব্যতিক্রম তিউতামস (Teutamus)- যাঁকে তিনি অন্য সবার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। যখন আমরা এ প্রশংসার কারণ খুঁজতে যাই তখন পাই তিউতামস বলেছিলেন, অধিকাংশ মানুষই মন্দ।
তিনি ভাবতেন একমাত্র বল প্রয়োগই নিজের মঙ্গলের জন্য কাজ করতে তাঁদের বাধ্য করবে যা ছিল মানুষজাতির প্রতি তাঁর ঘৃণার ফসল। তিনি বলতেনঃ প্রত্যেকটি পশুকেই চারণভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয় প্রহার করে, আরও বলতেনঃ গাধারা সোনার চাইতে খড়ই বেশি পছন্দ করে।
হেরাক্লিডস যুদ্ধে বিশ্বাসী ছিলেন, এটা ধারণা করা যেতে পারে। তিনি বলতেন, যুদ্ধই সবের জনক এবং সবার রাজা, যুদ্ধ কাউকে দেবতা করেছে, কাউকে করেছে মানুষ, কাউকে করেছে দাস এবং কাউকে স্বাধীন। আবার, যদি দেবতা মানুষের মধ্যে এই লড়াই মুছে যেত!-একথা বলে হোমের ভুল করেছেন। তিনি বুঝতে পারেননি যে, তিনি মহাবিশ্ব ধ্বংসের জন্য প্রার্থনা করছেন, কারণ তাঁর প্রার্থনা সাফল্যমণ্ডিত হলে সব জিনিসই শেষ হয়ে যাবে। এবং আরও এটা অবশ্য জ্ঞাতব্য যে, যুদ্ধ সব কিছুর মধ্যেই আছে এবং লড়াই-ই ন্যায়। সকল বস্তুই যুদ্ধের মাধ্যমে অস্তিত্বপ্রাপ্ত হয় এবং যুদ্ধের মধ্য দিয়েই বিনষ্ট হয়।
এক ধরনের কঠোর তপশ্চর্যার অহমিকা-অনেকটা নিটশের মতো ছিল তাঁর নীতিবোধে। তাঁর ধারণায় আত্মা অগ্নি এবং জলের একটি মিশ্রণ, অগ্নি এবং জলের একটি মিশ্রণ, অগ্নি উত্তম এবং জল অধম। যে আত্মায় অগ্নি অধিক তাকে তিনি বলেছেন শুষ্ক। শুষ্ক আত্মাই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং প্রাজ্ঞতম। আত্মাদের কাছে সিক্ত হওয়াই আনন্দের। একটি লোক পানোন্মত্ত হলে তাকে পথ দেখায় অজাতশ্মশ্রু একটি বালক-তারপর পদক্ষেপ অস্থির, কোথায় পা ফেলতে হবে জানে না, আত্মা তার সিক্ত। জল হয়ে যাওয়া হলো একটি আত্মার মৃত্যু। নিজের মনের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে লড়াই করা খুব শক্ত। সে তার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে আত্মিক মূল্যের বিনিময়ে। মানুষের সব আকাক্ষার পূরণ হওয়া তার পক্ষে মঙ্গলদায়ক নয়। বলা যেতে পারে হেরাক্লিডস আত্মনিয়ন্ত্রণের সাহায্যে ক্ষমতাশালী হওয়াকে মূল্য দিতেন এবং যে সমস্ত ভাবাবেগ মানুষকে তার মূল আকাক্ষা থেকে বিচ্যুত করে সেগুলোকে তিনি ঘৃণা করতেন।
তদানীন্তন ধর্ম, অন্ততপক্ষে বাকশীয় ধর্ম সম্পর্কে হেরাক্লিডসের মনোভাব ছিল প্রধানত বিরোধী কিন্তু এ বিরোধ বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদীর বিরোধ নয়। তাঁর নিজস্ব ধর্ম আছে এবং তিনি তদানীন্তন ধর্মতত্ত্বের অংশত ব্যাখ্যা করেছেন নিজের মতবাদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, অংশতি পরিত্যাগও করেছেন যথেষ্ট ঘৃণার সঙ্গে। তাঁকে বাকখীয় আখ্যা দেওয়া হয়েছে (Cornford দ্বারা) এবং অতীন্দ্রিয়বাদের ব্যাখ্যাতাও বলা হয়েছে। (Pfleiderer দ্বারা)। প্রাসঙ্গিক লেখাগুলো এই মতবাদ সমর্থন করে বলে আমার মনে হয় না। উদাহরণস্বরূপ, তিনি বলছেন? লোকে যে ধরনের অতীন্দ্রিয় আচার অভ্যাস করে সেগুলো অপবিত্র। এ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাঁর মনে হয়তো সম্ভাব্য এমন অতীন্দ্রিয়বাদ ছিল যেগুলো অপবিত্র নয়, তবে তদানীন্তন অতীন্দ্রিয়বাদীর চাইতে সম্পূর্ণ পৃথক। যে সমস্ত অতি সাধারণ লোক আত্মপ্রচার করে তাদের সম্পর্কে যদি তার অত্যন্ত ঘৃণা না থাকত তাহলে তিনি হয়তো ধর্মসংস্কারক হতেন।
নিম্নলিখিত বক্তব্যগুলো হেরাক্লিসের— যা আজও বর্তমান। এ থেকে তদানীন্তন ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে তার মনোভাব বুঝা যায়।
দিলফি-র দৈববাণীর যে দেবতা— তিনি কিছু প্রকাশও করেন না, কিছু গোপনও করেন না— শুধু ইঙ্গিত দেখিয়ে দেন।
এবং সিবিল (Sibyl)-এর থেকে উচ্চারিত আনন্দহীন প্রলাপ অনাড়ম্বর এবং সৌরভহীন। তাঁর কণ্ঠস্বর পৌঁছে যায় হাজার হাজার বছরের অধিক—তার অন্তর্বাসী দেবতাকে ধন্যবাদ।
হাদেস…এ আছে আত্মা দুর্গন্ধযুক্ত।
বৃহত্তর মৃত্যু আনে বৃহত্তম পুরস্কার। (এভাবে মৃতরা দেবত্বপ্রাপ্ত হয়)
নিশাচর (বেশ্যা), জাদুকর, বাকখস পূজারী এবং মদের জালার নারী পুরোহিত… এঁরা অতীন্দ্রিয়বাদ ব্যবসায়ী।
লোকে যে সমস্ত অতীন্দ্রিয়বাদ অভ্যাস করে সেগুলো অপবিত্র।
তারা এই দেবতাদের কাছে এমনভাবে প্রার্থনা করে যেন তারা কোনো মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন। অথচ তারা জানেন না কাকে দেবতা বলে কিংবা কাকে বীর বলে।
তারা যে শোভাযাত্রা করেন এবং লজ্জাস্কর লিঙ্গাত্মক গান করেন–সেগুলো যদি দিওনিসিয়স এর জন্য না হতো, তাহলে সেগুলো হতো অত্যন্ত নির্লজ্জ কাজ। কিন্তু হাদেস এবং দিওনিসিয়স অভিন্ন, দিওনিসিয়সের সম্মানেই তাঁরা প্রমত্ত হন এবং তাদের মদের জালার উৎসব হয়।
তাঁরা রক্ত মেখে নিজেদের অপবিত্র করে বৃথাই নিজেদের পবিত্র করেন…. ঠিক যেন কেউ কাদা মাড়িয়ে আবার কাদা দিয়েই পা পরিষ্কার করছেন। কাউকে এরকম করতে দেখলে লোকে ভাববে মানুষটা পাগল।
আগুনই আদিম উপাদান, তা থেকেই অন্য সব জিনিসের উৎপত্তি, এই ছিল হেরাক্লিডসের বিশ্বাস। পাঠকের মনে পড়বে … থালেস ভেবেছিলেন সবেরই সৃষ্টি জল থেকে। আনাক্সিমেনেস ভাবতেন, আদিম উপাদান বায়ু। হেরাক্লিডসের পছন্দ ছিল আগুন। শেষে এমপেদক্লেস (Empedocles) একজন রাজনীতিবিদের মতো একটা রফার প্রস্তাব দেন। ক্ষিতি, বায়ু, অগ্নি ও জল … এই চারটি উপাদানের কথা তিনি বলেন। আদিকালের রসায়নশাস্ত্র এখানে এসেই নীরব হয়। যতদিন পর্যন্ত না মুসলমান অপরসায়নবিদরা (alchemists) পরশমণি, অমৃত এবং নিকৃষ্ট ধাতুগুলোকে সোনায় রূপান্তরিত করার পদ্ধতি অনুসন্ধান করতে শুরু করেছেন ততদিন পর্যন্ত রসায়নশাস্ত্রের কোনো অগ্রগতি হয়নি।
হেরাক্লিসের অধিবিদ্যা বস্তুতম আধুনিককেও তুষ্ট করার মতো: গতিশীল: এ বিশ্ব সবার পক্ষে সমান, কোনো মানুষ কিংবা দেবতা এ বিশ্ব সৃষ্টি করেনি। বিশ্ব ছিল, এখন আছে এবং ভবিষ্যতে চিরকাল থাকবে…এ এক চিরজ্বলন্ত আগুন কোথাও নিভছে, কোথাও জ্বলছে।
আগুনের প্রথম রূপান্তর সমুদ্রে, সমুদ্রের অর্ধেক ক্ষিতি, অর্ধেক ঘূর্ণিঝড়। এরকম বিশ্বে নিরন্তর পরিবর্তনই আশা করা যায় আর এই অবিরত পরিবর্তনেই ছিল হেরাক্লিসের বিশ্বাস।
তাঁর আর একটি মতবাদ ছিল … তাঁর কাছে এর মূল্য নিরন্তর পরিবর্তনের চাইতে বেশি; এ মতবাদ ছিল বৈপরীত্য মিশ্রণের মতবাদ। তিনি বলেন, যার সঙ্গে পার্থক্য তার সঙ্গে কী করে ঐক্য হয় মানুষ জানে না। এ যেন বিপরীত বিততির (tension) সুর মেলানো বীণা এবং ছড়ের মতো। তার দ্বন্দ্বে বিশ্বাস এই তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত, তার কারণ, দ্বন্দ্বের ফলে বিপরীতের সমন্বয় ঘটে এবং উৎপন্ন হয় একটি গতি…..সেটাই সঙ্গতি (harmony)। বিশ্বের ঐক্য রয়েছে কিন্তু এই ঐক্যের উৎপত্তি অনৈক্য থেকেঃ
পূর্ণ এবং অপূর্ণের যুগল হয়….যা একসঙ্গে আকর্ষিত হয় এবং বিকর্ষিত হয়, যার সঙ্গতি আছে এবং যার সঙ্গতি নেই। সব বস্তু থেকেই এক .. এর উৎপত্তি এবং এক থেকেই সব বস্তুর উৎপত্তি।
অনেক সময় তিনি এমনভাবে বলেন যেন বৈচিত্র্যের চাইতে ঐক্যেরই গুরুত্ব বেশিঃ
ভালো এবং মন্দ একই।
ঈশ্বরের কাছে সবই ন্যায়, সবই ভালো, সবই সঠিক। মানুষ কিছু জিনিসকে ভুল, কিছু জিনিসকে সঠিক বলে।
উপরে যাওয়ার পথ এবং নিচে নামবার পথ এক এবং অভিন্ন।
ঈশ্বর দিন এবং রাত্রি, শীত এবং গ্রীষ্ম, যুদ্ধ এবং শান্তি, প্রাচুর্য এবং ক্ষুধা, কিন্তু তিনি আগুনের মতো নানা রূপ ধারণ করেন, যেমন, আগুনের সঙ্গে কোনো মশলা মেশালে সে মশলার স্বাদ-গন্ধ অনুসারে আগুনের নাম হয়।
তবে সমন্বিত হওয়ার মতো বৈপরীত্য না থাকলে ঐক্য থাকত না : আমাদের পক্ষে যা ভালো তা হলো বৈপরীত্য।
এই মতবাদে হেগেলের দর্শনের বীজ রয়েছে, সে দর্শনও বৈপরীত্যের সমন্বয় নিয়ে অগ্রসর হয়।
আনাক্সিমাস-এর অধিবিদ্যার মতো হেরাক্লিসের অধিবিদ্যাতেও মহাজাগতিক ন্যায়পরায়ণতার (cosmic justice) কল্পনের প্রাধান্য রয়েছে। এই ন্যায়পরায়ণতা
বৈপরীত্যের দ্বন্দ্ব- কোনো পক্ষকে সম্পূর্ণ বিজয়ী হতে দেয় না।
সব বস্তুই আগুনের বিনিময় এবং সব জিনিসের বিনিময়েই আগুন- ঠিক যেমন বস্তুর বিনিময়ে সোনা পাওয়া যায় এবং সোনার বিনিময়ে বস্তু।,
বায়ুর মৃত্যুতে আগুন বেঁচে থাকে। আগুনের মৃত্যুতে বায়ু বেঁচে থাকে, ক্ষিতির মৃত্যুতে জল বেঁচে থাকে, জলের মৃত্যুতে বেঁচে থাকে ক্ষিতি।
সূর্য তার মাত্রা অতিক্রম করবে না, যদি করে তাহলে ন্যায়ের পরিচারিকা। এরিনিসরা (Erinyes) তাকে ধরে ফেলবেন।
আমাদের জানতেই হবে যুদ্ধ সবার ভিতরেই আছে এবং দ্বন্দ্বই ন্যায়।
হেরাক্লিস বারবারই ঈশ্বরের কথা উল্লেখ করেছেন যিনি বহু দেবতাদের থেকে পৃথক। মানবিক পথের প্রজ্ঞার অভাব আছে কিন্তু ঈশ্বরের পথে তা নেই … ঈশ্বর মানুষকে শিশু বলেন, মানুষ যেমন শিশুকে বলে… প্রাজ্ঞতম ব্যক্তিটিও ঈশ্বরের তুলনায় যেন বাঁদর, ঠিক যেমন সুন্দরতম বাদর মানুষের তুলনায় কুশ্রী।
নিঃসন্দেহে ঈশ্বর হলেন মহাজাগতিক ন্যায়ের মূর্তরূপ।
হেরাক্লিসের মতগুলোর ভিতরে বিখ্যাততম হলো সব বস্তুর নিরন্তর পরিবর্তনশীলতা যা প্লাতনের (Plato) থিয়েতেতস (Theaetetus)-এ রয়েছে, তার শিষ্যরা এই মতবাদকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন।
একই নদীতে তুমি দুবার নামতে পার না, কারণ, নতুন জল সব সময় তোমার উপর বয়ে চলেছে।৩৯
সূর্য নিত্যই নতুন।
মনে করা হয়ে থাকে, ব্রহ্মাণ্ডের পরিবর্তনশীলতার প্রতি তাঁর বিশ্বাস এই বাক্যে প্রকাশ পেয়েছে সব বস্তুই বহমান, কিন্তু মনে হয় ওয়াশিংটনের বলা- বাবা, আমি তো মিথ্যা কথা বলতে পারব না এবং ওয়েলিংটনের বলা- সৈনিকরা ওঠো এবং আক্রমণ করো-বাক্য দুটির মতো হেরোক্লিসের এই বাক্য অপ্রমাণিত। প্লাতনের পূর্ববর্তী সমস্ত দার্শনিকদের মতো তাঁর বাক্যগুলোও উদ্ধৃতির মাধ্যমে জানা যায়, এই উদ্ধৃতিগুলো আবার করেছিলেন প্রধানত প্লাতন এবং আরিস্ততেলেস, তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল যুক্তিতর্ক দিয়ে এগুলোকে খণ্ডন করা। আধুনিক কোনো দার্শনিকের পরিচয় যদি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের বাদানুবাদের মাধ্যমে হয় তাহলে তার কী দশা হবে এই কথা ভাবলে প্রাক-সক্রাতেস দার্শনিকরা কত প্রশংসার যোগ্য তা মানতে হয়। তার কারণ, তাঁদের শক্ররা যে বিদ্বেষের বাষ্প বিস্তার করেছিলেন তার ভিতর দিয়েও সেই দার্শনিকদের মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। সে যাই হোক, প্রাতন এবং আরিস্ততেলেস একমত যে হেরাক্লিসের শিক্ষা ছিল, কিছুই চিরস্থায়ী নয়, সকলই ঘটমান (প্লাতন), এবং কিছুই দৃঢ়ভাবে স্থায়ীভাবে বর্তমান নয় (আরিস্ততেলেস)।
এই মতবাদে আবার ফিরে আসব যখন প্লাতন সম্পর্কে আলোচনা করব। প্লাতন এই মতবাদ খণ্ডন করতে খুবই উৎসুক। আপাতত এই বিষয়ে দর্শনশাস্ত্রের কী বক্তব্য সে অনুসন্ধান না করে শুধু বলব-কবিরা কী অনুভব করেছিলেন এবং বৈজ্ঞানিকদের শিক্ষা কী।
ধ্রুব-এর অনুসন্ধান করা মানুষের গভীরতম সহজাত প্রবৃত্তি। সেই প্রবৃত্তিই মানুষকে দর্শনশাস্ত্রের অভিমুখে নিয়ে গেছে। সন্দেহ নেই, এর উৎপত্তি মানুষের গৃহের প্রতি ভালোবাসা ও বিপদে নির্ভরতার আকাক্ষা থেকে। দেখা যায়-যাদের জীবন যত বিপদসঙ্কুল এ আকাঙ্ক্ষা তাদের ততই তীব্র। ধর্মে স্থিতির অনুসন্ধান দুই প্রকার- ঈশ্বর এবং অমরত্ব। ঈশ্বরে পরিবর্তনশীল কিছু নেই, এমনকি নড়াচড়ার ছায়ামাত্র নেই; মৃত্যুর পরবর্তী জীবন অনন্ত এবং পরিবর্তনহীন। ঊনবিংশ শতাব্দীর হর্ষোফুল্ল মনোভাব মানুষকে এই সমস্ত স্থির কল্পনের বিরুদ্ধে নিয়ে গিয়েছে এবং আধুনিক উদার ধর্মতত্ত্ব বিশ্বাস করে-স্বর্গেও প্রগতি রয়েছে এবং দেবত্বেরও বিবর্তন হয়। কিন্তু এই কল্পনেও চিরস্থায়ী কিছু রয়েছে, যেমন প্রগতি নিজে এবং তার ধ্রুব লক্ষ্য। আবার একপশলা বিপর্যয় সম্ভবত মানুষের আশা ভরসাকে প্রাক্তন অতি-পার্থিবে ফিরিয়ে আনবেঃ পৃথিবীতে জীবন হতাশাপূর্ণ হলে, একমাত্র স্বর্গেই শান্তির অনুসন্ধান করা যায়।
ভালোবাসার সব বস্তুই কাল হরণ করে বলে কবিরা দুঃখ করেছেন বলেন–
উদ্ধত যৌবনকে বিদ্ধ করে কাল,
সুন্দরের ললাটে এঁকে দেয় বলিরেখা,
প্রকৃতির দুর্লভ সত্য কালের আহার,
যা থাকে তা শুধু অপেক্ষা করে কাল- খড়গের।
এর পরপরই তারা বলতে দ্বিধা করেন না যে তাঁদের নিজেদের কবিতা অক্ষয় :
তবুও আশা কালের বক্ষে আমার কাব্য থাকবে,
থাক না কালের করাল হাত, তবুও গাইব তোমার গুণ।
আর এটাই হলো শুধুমাত্র প্রচলিত সাহিত্যিক দম্ভ।
কালের প্রবাহে সবই ক্ষণস্থায়ী- দার্শনিকতাপ্রবণ অতীন্দ্রিয়বাদীরা এ কথা অস্বীকার করতে অপারগ হয়ে এমন এক কল্পন আবিষ্কার করেছেন যা অন্তহীন কালে চিরস্থায়ী নয়, তা কালের ক্রিয়ার বাইরে। কোনো কোনো ধর্মতাত্ত্বিকের, যেমন ডিন ইঙ্গে (Dean Inge)-র মতে, অনন্ত জীবনের অর্থ ভবিষ্যকালের প্রতিটি মুহূর্তে অস্তিত্বশীল থাকা নয়, তার অর্থ কাল নিরপেক্ষ অস্তিত্ব। সে অস্তিত্বে কোনো পূর্বাপর নেই, সুতরাং পরিবর্তনের কোনো যৌক্তিক সম্ভাবনাও নেই। ভগান (Vaughan) এ দৃষ্টিভঙ্গি কাব্যে প্রকাশ করেছেনঃ
কাল রাতে আমি অনাদি অনন্ত দেখেছি,
যে শুদ্ধ অনন্ত আলোকের বিরাট একটা চক্র,
শান্ত, উজ্বল;
তাকে ঘিরে তার নিচে রয়েছে কাল, ঘণ্টা, দিন আর বছর,
বহু গোলকের তাড়নায়
বিরাট ছায়ার মতো চলমান; সেই ছায়ায় নিক্ষিপ্ত হলো
বিশ্ব এবং তার সর্বস্ব।
অনেক বিখ্যাত দর্শনতন্ত্র এই কল্পন শান্ত গদ্যে বিবৃত করার চেষ্টা করেছে, এমন যুক্তি বিকশিত করেছে যা ধৈর্যসহকারে অনুধাবন করলে আমরা সে কল্পন মানতে বাধ্য হব।
পরিবর্তনে বিশ্বাস সত্ত্বেও হেরাক্লিস নিজে চিরন্তন কিছু একটা বিশ্বাস করেছিলেন। (অশেষ স্থায়িত্বের বিপরীতে) অনাদি অনন্তের কল্পন এসেছে পার্মেনিদেস (Parmenides) এর কাছ থেকে, হেরাক্লিডসে এ কল্পন নেই কিন্তু রয়েছে মৃত্যুহীন কেন্দ্রীয় আগুন : এ বিশ্ব চিরকাল ছিল, এখন আছে এবং ভবিষ্যতে থাকবে-থাকবে এই চিরজীবন্ত আগুন। কিন্তু আগুন এমন একটা জিনিস যা অবিরত পরিবর্তিত হচ্ছে। এবং এর স্থায়িত্ব একটি বস্তুর স্থায়িত্ব নয়, একটি পদ্ধতির স্থায়িত্ব-যদিও এই মত হেরাক্লিসের উপর আরোপ করা ঠিক হবে না।
এইসব পরিবর্তনশীল পরিঘটনার মধ্যে দর্শনশাস্ত্রের মতো বিজ্ঞানও নিরন্তর পরিবর্তনের মতবাদ থেকে পলায়নের জন্য একটি চিরস্থায়ী ভিত্তিমূল (Substratum) খুঁজেছে। মনে হয়েছিল রসায়নশাস্ত্র এই ইচ্ছা পূর্ণ করছে। দেখা গিয়েছিল আপাতদৃষ্টিতে আগুন ধ্বংসকারী মনে হলেও আসলে আগুন বস্তুর রূপের পরিবর্তন করে, মৌলিক উপাদনগুলোর পুনর্বিন্যাস হয়। দহনের (combustion) পূর্বে সে পরমাণুগুলো ছিল দহন ক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার পরও তার প্রতিটি পরমাণুরই অস্তিত্ব থাকে। সুতরাং অনুমান করা হয়েছিল পরমাণু কখনোই ধ্বংস হয় না এবং ভৌত জগতের প্রতিটি পরিবর্তনই শুধুমাত্র স্থায়ী উপাদানগুলোর পুনর্বিন্যাস। তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত এই মতবাদই প্রতিষ্ঠিত ছিল কিন্তু তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারের পর দেখা গেল পরমাণুগুলো ভঙ্গুর।
পদার্থবিদ্যাবিদরা বিন্দুমাত্র ভয় না পেয়ে নতুন এবং ক্ষুদ্রতর একক আবিষ্কার করলেন- সেগুলোর নাম দিলেন ইলেকট্রন ও প্রোটন। এগুলো দিয়েই পরমাণু গঠিত হয় এবং কয়েক বছর পর্যন্ত অনুমান করা গিয়েছিল পূর্বে পরমাণুতে আরোপিত অক্ষয়ত্ব এই এককগুলোতে আরোপ করা যাবে। দুর্ভাগ্যক্রমে দেখা গেল প্রোটন এবং ইলেকট্রনে সংঘর্ষ হয়ে বিস্ফোরণ হতে পারে, তার ফলে কিন্তু নতুন পদার্থের সৃষ্টি হয় না, সৃষ্টি হয় শক্তি-সে শক্তির তরঙ্গ আলোক তরঙ্গের গতিতে মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। চিরস্থায়ী বস্তুরূপে পদার্থের স্থানে স্থাপিত হলো শক্তি। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিতে শক্তি পদার্থের মতো বস্তুর সংস্কৃত (refinement) রূপ নয়, শক্তি শুধু ভৌত পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য মাত্র। কল্পনায় শক্তিকে হয়তো হেরাক্লিসের আগুনের সঙ্গে অভিন্ন ভাবা যেতে পারে কিন্তু হেরাক্লিডসের আগুন হলো দহন, দহনীয় নয়। দাহ্য পদার্থ (দহনীয়) আধুনিক পদার্থবিদ্যা থেকে অদৃশ্য হয়েছে।
ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ-এ গেলে দেখা যায়, মহাকাশের বস্তুপিণ্ডগুলোকে জ্যোতির্বিজ্ঞান আর চিরস্থায়ী মনে করে না। গ্রহগুলো হয়েছে সূর্য থেকে, সূর্য হয়েছে নীহারিকা (nebula) থেকে। এরা কিছুকাল রয়েছে, আরও কিছুকাল থাকবে কিন্তু আগে হোক পরে হোক-হয়তো এক লক্ষ কোটি বছরে এগুলোতে বিস্ফোরণ হবে এবং সমস্ত গ্রহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অন্তত তাই বলেন। হয়তো অন্তিম দিন যখন ঘনিয়ে আসবে তখন তাঁরা নিজেদের গণনায় কোনো ভুল আবিষ্কার করতে পারবেন।
হেরাক্লিডস নিরন্তর পরিবর্তনের মতবাদ দ্বারা যে শিক্ষা দিয়েছেন, তা বেদনাদায়ক এবং দেখা গেল তাকে অস্বীকার করার মতো কিছু বিজ্ঞানে নেই। বিজ্ঞান যে আশাকে নির্বাপিত করেছে তাকে পুনর্জাগরিত করা দার্শনিকদের প্রধান উচ্চাকাঙ্ক্ষা। সুতরাং দার্শনিকরা খুব অধ্যবসায়ের সঙ্গে এমন জিনিস খুঁজেছেন বা কালসাম্রাজ্যের অধীন নয়। এ অনুসন্ধান শুরু হয়েছে পার্মেনিদেসের সঙ্গে সঙ্গে।