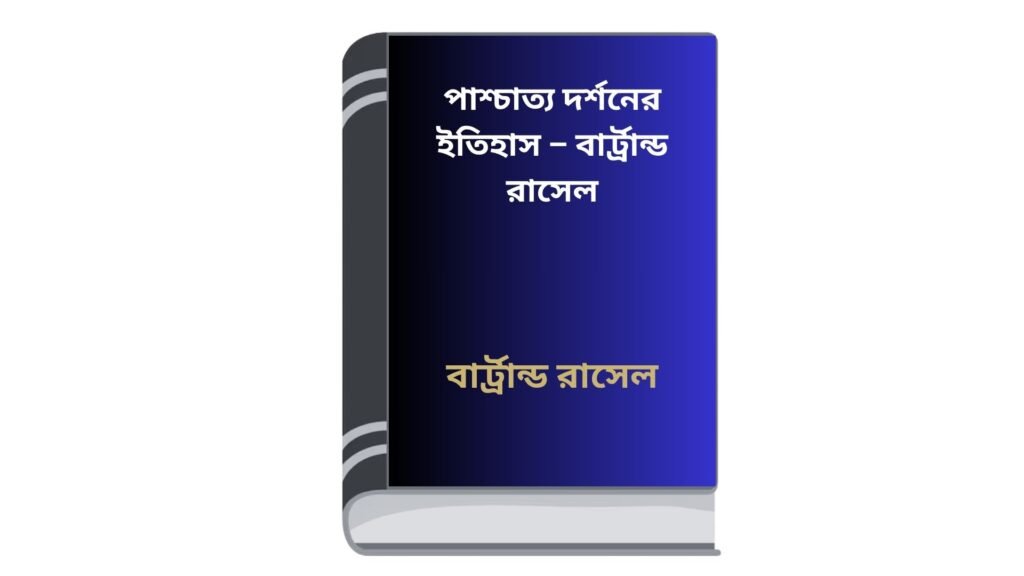০৬. এমপেদক্লেস
৬. এমপেদক্লেস
দার্শনিক, দিব্যপুরুষ, বৈজ্ঞানিক এবং ভণ্ড (charlaton)-এর মিশ্রণ আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি পুথাগরসে, তারই আর একটি পূর্ণ দৃষ্টান্ত এমপেদক্লেস (Empedocles)। তাঁর জীবনকাল ৪৪০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি, সুতরাং তিনি ছিলেন পার্মেনিদেসের বয়োকনিষ্ঠ সমসাময়িক। যদিও তাঁর মতবাদের সঙ্গে বেশি মিল ছিল হেরাক্লিসের মতবাদের। তিনি সিসিলির দক্ষিণ উপকূলের আক্রাগাস (Acragas)-এর নাগরিক ছিলেন। তিনি ছিলেন গণতান্ত্রিকতাবাদী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং একই সঙ্গে নিজেকে দেবতা বলে দাবি করতেন। অধিকাংশ গ্রিক নগরগুলোতে, বিশেষ করে সিসিলির নগরগুলোতে গণতন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্রের নিরবচ্ছিন্ন দ্বন্দ্ব চলত। পরাজয়ের মুহূর্তে বিজিত দলের নেতাকে হয় নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হতো, নয় দেওয়া হতো মৃত্যুদণ্ড। যাঁদের নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হতো তারা গ্রিসের শত্রুদের সঙ্গে অর্থাৎ পূর্বদিকে পারস্য এবং পশ্চিমদিকে কার্থেজের সঙ্গে আলোচনায় বসতে দ্বিধা করতেন না যথাকালে এমপেদক্লেসও নির্বাসিত হলেন কিন্তু মনে হয় নির্বাসিত হওয়ার পর ষড়যন্ত্রকারী উদ্বাস্তুর জীবনের চাইতে ঋষির কর্মজীবনই তাঁর পছন্দ ছিল। সম্ভবত যৌবনে তিনি অল্পবিস্তর অফীয় ছিলেন। নির্বাসনের আগে বিজ্ঞান এবং রাজনীতির একটা সমন্বয় করেছিলেন এবং উদ্বাস্তু হওয়ার পরে শুধু শেষ জীবনেই তিনি দিব্যপুরুষ হয়েছিলেন।
এমপেদক্লেস সম্পর্কে বহু কাহিনি প্রচলিত। মনে করা হতো তিনি বহু অলৌকিক কাজ করেছেন কিংবা এমন কাজ করতেন যা অলৌকিক মনে হতো। এ কাজ তিনি করতেন জাদুবিদ্যার সাহায্যে আবার কখনো তার বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাহায্যে। আমরা শুনেছি-তিনি বায়ুপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন। ত্রিশ দিন পরে আপাত মৃত এক মহিলাকে প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। কথিত আছে, পরিশেষে তিনি নিজেকে দেবতা প্রমাণ করার জন্য এনা (Etna)-এর গর্ভে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। কবির ভাষায়ঃ
ব্যাকুল আত্মা, মহা এমপেদক্লেস,
ঝাঁপ দিলেন এতনায়–দগ্ধ হলেন সম্পূর্ণ।
ম্যাথু আর্নল্ড (Mathew Arnold) এই বিষয়ে একটি কবিতা লিখেছিলেন কিন্তু সে কবিতা তাঁর নিকৃষ্টতম কবিতা হলেও তাতে উপরোল্লিখিত এই পংক্তি দুটি নেই।
এমপেদক্লেসও পার্মেনিদেসের মতো লিখতেন ছন্দে। লুক্ৰেতিয়ুসের (Lucretius) উপরেও তার প্রভাব ছিল। লুক্রেতিয়ুস তাঁর কবি প্রতিভার উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন কিন্তু এবিষয়ে মতভেদ ছিল। তাঁর রচনার মাত্র কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকায় তাঁর কবি প্রতিভা সম্পর্কে সংশয় নিরসন হয় না।
তাঁর বিজ্ঞান এবং তাঁর ধর্ম সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন, কারণ, এদের পরস্পরের ভিতরে কোনো সঙ্গতি নেই। আমি প্রথমে বিচার করব তার বিজ্ঞান, তারপর তার দর্শন এবং সবশেষে তার ধর্ম।
বায়ুকে স্বতন্ত্ররূপে আবিষ্কার ছিল বিজ্ঞানে তাঁর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। একটি বালতি অথবা এ জাতীয় পত্র (vessel) উল্টো করে জলে ডোবালে তাতে জল ঢোকে না-এটা লক্ষ্য করে তিনি এর আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি বলেনঃ
ঝকমকে পেতলের একটা জলঘড়ি নিয়ে খেলা করবার সময় কোনো মেয়ে যখন ঘড়ির ছিদ্রগুলো তার স্থির হাত দিয়ে ঢেকে জলঘড়িটাকে রূপোলি জলে ডোবায় তখন জলস্রোত পাত্রে ঢোকে না, জলটা সরে গিয়ে ঘড়িকে স্থান দেয় কিন্তু জলটা ঘড়ির ভিতরে ঢুকতে পারে না। যতক্ষণ না মেয়েটি হাত সরিয়ে নেয় ততক্ষণ জল ঘড়ির বাইরেই থাকে, হাত সরিয়ে নিলে হাওয়া বেরিয়ে গিয়ে সমপরিমাণ জল ভিতরে ঢোকে।
শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাখ্যা সম্পর্কে এই লেখাটি পাওয়া গেছে।
তিনি অপকেন্দ্রিক বলের অন্তত একটি উদাহরণও আবিষ্কার করছিলেন? সেটা হলো, এক পেয়ালা জলকে যদি একটি দড়ির ডগায় বেঁধে ঘোরানো যায় তবে জলটা বেরিয়ে আসে না।
উদ্ভিদের লিঙ্গভেদের অস্তিত্ব তিনি জানতেন এবং বিবর্তন ও সবচাইতে উপযুক্ত হয়ে বেঁচে থাকার একটি তত্ত্ব তাঁর ছিল (খানিকটা কল্পনাভিত্তিক-এটা অস্বীকার করার উপায় নেই)। আদিতে, প্রথমে অগণিত উপজাতির মরণশীল জীব চতুর্দিকে বিস্তৃত ছিল, তাদের আকার ছিল নানারকম- দেখলেও অবাক লাগে। মাথা ছিল গলা ছিল না, হাত ছিল কাঁধ ছিল না, চোখ ছিল কপাল ছিল না, মিলনাকাঙ্ক্ষী একাধিক একক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিল। এগুলো যেমন সুযোগ মিলল তেমনভাবে জুড়ে গেল; এমন জন্তু ছিল যাদের পদক্ষেপ অস্থির কিন্তু তাদের হাতের সংখ্যা অগণিত, কিছু এমন জন্তু ছিল যাদের মুখ আর বুক বিভিন্ন অভিমুখী, কিছু জন্তুর ছিল ষাঁড়ের মতো ধড় কিন্তু মানুষের মতো মুখ আবার কিছু জন্তুর ছিল ষাঁড়ের মতো মুখ কিন্তু মানুষের ধড়। উভলিঙ্গ প্রাণী ছিল, তাদের স্বভাব ছিল স্ত্রী এবং পুরুষের সমন্বয় কিন্তু তারা নিঃসন্তান। শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র কয়েকটি গঠনই বেঁচে যায়।
জ্যোতির্বিদ্যার বিষয় : চাঁদ যে প্রতিফলিত আলোকে উজ্জ্বল এটা তিনি জানতেন, তার ধারণা ছিল সূর্য সম্পর্কে এ কথা সতি; তিনি বলেছিলেন যে, আলোকের গমনাগমনে সময় লাগে কিন্তু সে সময় এতই কম যে আমরা বুঝতে পারি না। পৃথিবী এবং সূর্যের মাঝখানে চাঁদ এসে পড়ার ফলে যে সূর্যগ্রহণ হয় এ তথ্য তিনি জানতেন, মনে হয় এটা তিনি শিখেছিলেন আনাক্সাগরসের (Anxagoras) কাছ থেকে।
তিনি ছিলেন ইতালীয় চিকিৎসাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং সেই বিদ্যালয় থেকে যে ইতালীয় চিকিৎসাবিদ্যালয়ের উদ্ভব তা প্লাতন এবং আরিস্ততেলেস উভয়কে প্রভাবিত করেছে। বার্ণেট (পৃষ্ঠা ২৩৪)-এর মতে এ বিদ্যালয় বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক চিন্তার সম্পূর্ণ প্রবণতাকে প্রভাবিত করেছে।
এ থেকে বোঝা যায় তাঁর যুগের বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রাণশক্তি। গ্রিসের পরবর্তী যুগ কখনোই এর সমকক্ষ হতে পারেনি।
এখন আমি তাঁর সৃষ্টি তত্ত্ব (cosmology) আলোচনা করব। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ক্ষিতি, বায়ু, অগ্নি এবং জল- এই চারটি মৌলিক উপাদানকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন (যদিও তিনি মৌলিক উপাদান শব্দটি ব্যবহার করেননি)। এই উপাদানের প্রতিটিই চিরস্থায়ী কিন্তু এগুলো বিভিন্ন অনুপাতে মিশ্রিত হয়ে পৃথিবীতে দৃষ্ট সমস্ত পরিবর্তনশীল জটিল বস্তু উৎপন্ন করতে পারত। এগুলোর সমন্বয় হয় প্রেমে এবং বিচ্ছিন্ন হয় দ্বন্দ্বে। এমপেদক্লেসের কাছে ক্ষিতি, অগ্নি, বায়ু এবং জলের মতোই প্রেম এবং দ্বন্দ্ব একই স্তরের আদিম পদার্থ ছিল। এমন সময় ছিল যখন প্রেমই ছিল ঊর্ধ্বগামী আবার এমন সময় ছিল যখন দ্বন্দ্বই ছিল বেশি শক্তিশালী। এমন একটা স্বর্ণযুগ ছিল যখন প্রেম সম্পূর্ণ বিজয়ী ছিল। সে যুগে মানুষেরা শুধু সিপ্রিয়ান (Cyprian-সাইপ্রাসের অধিবাসী) আফ্রদিতে (১২৮ পৃষ্ঠা থেকে)-র পূজা করতেন। পৃথিবীর পরিবর্তন কোনো উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, নিয়ন্ত্রিত হয় শুধুমাত্র আপতন এবং প্রয়োজনের দ্বারা। একটা চক্র রয়েছে- প্রেম যখন উপাদানগুলোকে নিবিড়ভাবে মিশিয়ে দিয়েছেন দ্বন্দ্ব তখন তাদের আবার ধীরে ধীরে পৃথক করেছে: দ্বন্দ্বের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর প্রেম তাদের ধীরে ধীরে পুনর্মিলিতি করে। সুতরাং প্রত্যেকটি যৌগ বস্তুই অস্থায়ী, শুধুমাত্র মৌলিক উপাদানগুলো এবং প্রেম ও দ্বন্দ্ব চিরস্থায়ী।
হেরাক্লিডসের সঙ্গে একটা সাদৃশ্য রয়েছে কিন্তু একটু নমনীয়, কারণ, শুধুমাত্র দ্বন্দ্ব একা নয়, প্রেম এবং দ্বন্দ্ব যুক্তভাবে পরিবর্তন আনে। সফিস্ট (Sophist-২৪২)-এ হেরাক্লিস এবং এমপেদক্রেসকে প্লাতন যুক্ত করেছেন।
কিন্তু ইওনীয়-র চিন্তক এবং ইদানীয়কালে কিছু সিসিলীয় চিন্তক রয়েছেন, তাঁদের সিদ্ধান্ত- দুটি তত্ত্বকে (একের এবং বহুর) সংযুক্ত করাই অধিক নিরাপদ। বলা উচিত সত্তা এক এবং বহু ও এরা পরস্পরের সঙ্গে শত্রুতা ও বন্ধুত্বের দ্বারা সংযুক্ত- তারা অবিরত বিচ্ছিন্ন হচ্ছে এবং মিলিত হচ্ছে। কঠোরতর চিন্তক দৃঢ়তার সঙ্গে এইরকমই বলেন কিন্তু যারা একটু নমনীয় তারা অবিরাম দ্বন্দ্ব এবং শান্তির উপরে জোর দেন না কিন্তু শৈথিল্য এবং পর্যানুবৃত্তি মেনে নেন। অনেক সময় শান্তি এবং ঐক্য আফ্রদিতের ছত্রছায়ায় বিরাজ করে তারপরই আবার দ্বন্দ্বনীতি অনুসারে শুরু হয় বহুত্ব এবং যুদ্ধ।
পৃথিবী একটি গোলক-এটা এমপেদক্লেসেরই মত। স্বর্ণযুগে দ্বন্দ্ব ছিল বাইরে এবং প্রেম ছিল অন্তরে। তারপর আস্তে আস্তে দ্বন্দ্ব প্রবেশ করল এবং প্রেম বিতাড়িত হলো। তারপর নিকৃষ্টতম অবস্থায় দ্বন্দ্ব সম্পূর্ণ ভিতরে থাকবে এবং প্রেম থাকবে গোলকের সম্পূর্ণ বাইরে। তারপর কোনো এক কারণে- যা ঠিক স্পষ্ট নয়- একটি বিপরীতমুখী গতি শুরু হয় এবং স্বর্ণ যুগ ফিরে আসে কিন্তু সেটাও চিরস্থায়ী হয় না। এই সম্পূর্ণ চক্রের পুনবৃত্তি হয়। ভাবা যেতে পারে যে, যে কোনো চরম অবস্থা চিরস্থায়ী হবে কিন্তু এমপেদক্লেসের দৃষ্টিভঙ্গি তা নয়। তিনি পার্মেনিদেসের যুক্তির ভিত্তিতে গতিকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন এবং কোনো স্তরেই অপরিবর্তনীয় ব্রহ্মাণ্ডে পৌঁছানোর ইচ্ছা তাঁর ছিল না।
ধর্ম বিষয়ে এমপেদক্লেসের মত প্রধানত পুথাগোরীয়। যতদূর সম্ভব পুথাগরস সম্পর্কেই একটি ছিন্নপত্রে (fragment) বলা হয়েছে। তাদের ভিতরে একজন ছিলেন অসাধারণ জ্ঞানী, জ্ঞানগর্ভ প্রতিটি কাজে তিনি ছিলেন নিপুণ, প্রজ্ঞার সর্বোত্তম সম্পদ তিনি জয় করেছিলেন। যখনই তিনি অখণ্ড মনোযোগে চেষ্টা করেছেন তখনই তিনি অতি সহজে সব জিনিসের সবকিছু দেখতে পেয়েছেন তার বিস্তার মানুষের দশ কিংবা বিশ জীবনকাল, যাই হোক না কেন। আগেই বলা হয়েছে স্বর্ণযুগে মানুষেরা শুধুমাত্র আফ্রাদতের পূজা করতেন, পূজা বেদী ষাঁড়ের খুঁটি রক্তের পুতিগন্ধে ভরে যেত না বরং মানুষ তখন হত্যা করে সুন্দর অঙ্গগুলো ছিঁড়ে খাওয়াকে নিদারুণ ঘৃণা করত।
এক সময় তিনি নিজের দেবত্ব সম্পর্কে উচ্ছ্বসিতভাবে বলেছেনঃ
বন্ধুগণ, আপনারা যারা আক্রাগাস-এর হলুদ পাথরের উপরের মহানগরীর নগর দুর্গের কাছে থাকেন ও সুকর্মে ব্যস্ত, যারা অপরিচিতদের সম্মান করেন, নিচ ব্যবহারে যারা অজ্ঞতারা সবাই অভিবাদন গ্রহণ করুন। আমি অমর দেবতা, এসেছি আপনাদের ভিতরে। মরজীব আমি নই, ফিতের মুকুট আর ফুলের মালায় যথাযোগ্য ভক্তি পাব। আমার পোশাকে এগুলো নিয়ে নগরগুলোতে আমি যখন প্রবেশ করি তখন শ্রদ্ধা করে সবাই, অগণিত লোক আমায় অনুসরণ করে। তারা প্রশ্ন করে-কোনটা লাভের পথ। কেউ চায় দৈববাণী আবার যারা দিনের পর দিন রোগ যন্ত্রণায় ভুগেছে তারা আমার কাছে শুনতে চায় আরোগ্যের বাণী…। কিন্তু কেন আমি এ কথা বলব? আমি যে মরণশীল, বিনাশশীল মানুষের উর্ধ্বে-সেটা কি এমন বেশি কিছু?
আবার অন্য একসময় তিনি নিজেকে মনে করেছেন অত্যন্ত পাপী, পাপাঁচরণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করছেন?
ভাগ্যের একটা দৈববাণী আছে- দেবতাদের একটা প্রাচীন বিধি। যে বিধি চিরন্তন, বৃহৎ প্রতিজ্ঞা দিয়ে কঠিনভাবে বদ্ধ, সে বিধিতে দিনের দৈর্ঘ্যের অধিকারী কোনো দেব মানবের আত্মা যখনই নিজের হাতকে রক্ত দিয়ে কলঙ্কিত করার পাপ করেছেন কিংবা দ্বন্দ্বকে অনুসরণ করেছেন এবং মিথ্যাকে শপথ করেছেন, তখন তাকে পুণ্যাত্মাদের বাসভূমি থেকে দূরে ঘুরে বেড়াতে হবে তিনবার প্রতিবার দশ হাজার বছর ধরে। এই সময় তাঁকে নানা মরজীবরূপে জন্ম নিতে হবে, এক ক্লান্তিকর জীবন থেকে অন্য এক ক্লান্তিকর জীবনে যেতে হবে। কারণ, শক্তিমান বায়ু তাঁকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে, সমুদ্র আবার তাকে উৎসর্জন করে শুষ্ক পৃথিবীতে, পৃথিবী তাঁকে নিক্ষেপ করে জ্বলন্ত সূর্যের কিরণে, সূর্য আবার তাকে নিক্ষেপ করে বায়ুর ঘূর্ণিস্রোতে। একজনের কাছ থেকে আর একজনের কাছে যান কিন্তু সকলেই তাকে বর্জন করে। এদেরই একজন আমি, নির্বাসিত এবং দেবতাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভ্রমণ করছি, কারণ আমি এক নির্বোধ দ্বন্দ্বে বিশ্বাস স্থাপন করেছি।
কী তার পাপ ছিল তা আমরা জানি না, হয়তো যাকে আমরা খুব গর্হিত মনে করি তেমনি কিছু নয়। কারণ তিনি বলছেন :
হায়, আমি গোগ্রাসে গেলার মতো মন্দ কাজ করার আগেই নির্মম মৃত্যুদিন কেন আমাকে ধ্বংস করল না! হায় রে আমার দুঃখ! …।
লরেল গাছের পাতা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকুন…।
হতভাগা একেবারেই হতভাগা। তোমরা শিম (beans) থেকে হাত সরিয়ে রাখো!
সুতরাং হয়তো লরেল পাতা চিবোনো কিংবা গোগ্রাসে শিম খাওয়ার মতো গর্হিত কিছু তিনি করেননি।
প্লাতনের লেখার বিখ্যাততম অংশে তিনি এই পৃথিবীকে একটি গুহার সঙ্গে তুলনা করেছেন, সেই গুহায় ঊর্ধ্বে অবস্থিত এক উজ্জ্বল বিশ্বের বাস্তব পদার্থের ছায়ামাত্র দেখতে পাই। এই মতবাদের পূর্বাভাস আমরা এমপেদক্লেস-এ পাই। এর উৎপত্তি অীয় শিক্ষা থেকে।
কিন্তু কেউ আছেন যারা সম্ভবত বহু জন্ম পাপ করেননি, তাঁরা দেবতাদের সাহচর্যে অনন্ত শান্তিলাভ করেন?
কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা মরণশীলদের ভিতরে দেখা দেন- দিব্যপুরুষ, সংগীত রচয়িতা, চিকিৎসক এবং রাজপুত্ররূপে। তারপর তারা সম্মানের উচ্চ শিখরে দেবতারূপে আরোহণ করেন, তারা অংশীদার হন দেবতাদের গৃহাগ্নির (hearth), তখন তাঁরা মানবিক দুঃখ থেকে মুক্ত, নিয়তি থেকে নিরাপদ এবং আঘাতের উর্ধ্বে।
মনে হয় এগুলোর ভিতরে এমন বিশেষ কিছু নেই যা অফীয়রা এবং পুথাগোরীয়রা আগে থেকে শিক্ষা দেননি।
বিজ্ঞানের বাইরে এমপেদক্লেসের মৌলিকত্ব দেখা যায় চারটি উপাদানের মতবাদে এবং পরিবর্তন ব্যাখ্যার জন্য প্রেম এবং দ্বন্দ্ব-এই দুটি তত্ত্বের ব্যবহারে।
তিনি অদ্বৈতবাদ (monism) বর্জন করেছিলেন, বিশ্বাস করতেন প্রকৃতির গতি নিয়ন্ত্রিত হয় আপতন এবং প্রয়োজনের দ্বারা, কোনো উদ্দেশ্যের দ্বারা নয়। এই সমস্ত দিক থেকে পার্মেনিদেস, প্লাতন (Plato) এবং আরিস্ততেলেসের তুলনায় তাঁর দর্শন ছিল অনেক বেশি বিজ্ঞানমুখী। অন্য দিক থেকে তিনি তদানীন্তন কুসংস্কারগুলো মেনে নিয়েছিলেন এ কথা সত্যি কিন্তু এদিক দিয়ে তিনি আধুনিক অনেক বৈজ্ঞানিকদের চাইতে মন্দ নন।