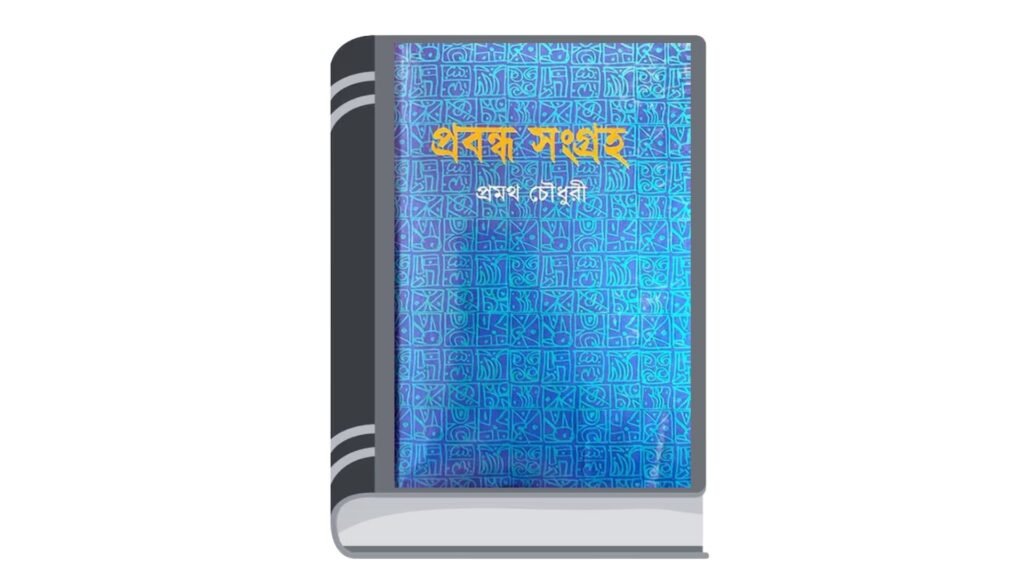মহাভারত ও গীতা
দেশপূজ্য ও লোকমান্য স্বর্গীয় বালগঙ্গাধর তিলক মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতার একখানি বিরাট ভাষ্য রচনা করেছেন, এবং মহাত্মা তিলকের অনুরোধে স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সে গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেছেন।১ সে ভাষ্য যে কত বিরাট তার ইয়ত্তা সকলে এই থেকেই করতে পারবেন যে, গীতার সপ্ত শত শ্লোকের মর্ম প্রায় সপ্তবিংশতি সহস্র ছত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ ভাষ্য এত বিশাল হবার কারণ এই যে, এতে বেদ উপনিষদ্ ব্রাহ্মণ নিরুক্ত ব্যাকরণ ছন্দ জ্যোতিষ পুরাণ ইতিহাস কাব্য দর্শন প্রভৃতি সমগ্র সংস্কৃত শাস্ত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সুবিচার করা হয়েছে। মহাত্মা তিলক এ গ্রন্থে যে বিপুল শাস্ত্রজ্ঞান, যে সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, তা যথার্থই অপূর্ব। সমগ্র মহাভারতের নৈলকণ্ঠীয় ভাষ্যও, আমার বিশ্বাস, পরিমাণে এর চাইতে ছোটো। তাইতে মনে হয় যে, এ ভাষ্য মহাত্মা তিলক প্রাকৃতে না লিখে সংস্কৃতে লিখলেই ভালো করতেন। কারণ এ গ্রন্থের পারগামী হতে পারেন শুধু সর্বশাস্ত্রের পারগামী পণ্ডিতজনমাত্র, আমাদের মতো সাধারণ লোক এ গ্রন্থে প্রবেশ করা মাত্রই বলতে বাধ্য হবে যে
ন হি পারং প্রপশ্যামি গ্রন্থস্যাস্য কথঞ্চন।
সমুদ্রস্যাস্য মহতো ভুজাভ্যাং প্রতরন্নরঃ ॥২
[১ . শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারহস্য। অথবা কর্মযোগশাস্ত্র। কলিকাতা, ১৯২৪ খ্ৰী।
২. মহাভারতের উপরোক্ত শ্লোকের আমি কেবল একটি শব্দ বদলে দিয়েছি, ‘দুঃখস্যাস্য’ পরিবর্তে ‘গ্রন্থস্যাস্য’ বসিয়ে দিয়েছি। আশা করি, তাতে অর্থের কোনো ক্ষতি হয় নি।]
মহাত্মা তিলক এ গ্রন্থের নাম দিয়েছেন কর্মযোগ। কেননা তিনি ঐ সুবিস্তৃত বিচারের দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, গীতা কর্মত্যাগের শিক্ষা দেয় না, শিক্ষা দেয় কর্মযোগের। আর যোগ মানে যে ‘কর্মসূ কৌশলং’, এ কথা তো স্বয়ং বাসুদেব গোড়াতেই অর্জুনকে বলেছেন। এই ব্যাখ্যাসূত্রে আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল। নীলকণ্ঠ গীতার ব্যাখ্যা আরম্ভ করেছেন এই ক’টি কথা বলে—
প্রণম্য ভগবৎপাদান্ শ্রীধরাদীংশ্চ সদ্গুরু
সম্প্রদায়ানুসারেণ গীতাব্যাখ্যাং সমারভে ॥
নীলকণ্ঠ অতি সাদা ভাবে স্বকীয় ব্যাখ্যা সম্বন্ধে যে কথা মুখ ফুটে বলেছেন, গীতার সকল টীকাকারই সে কথা স্পষ্ট করে না বললেও চাপা দিতে পারেন না। সকলেই স্বসম্প্রদায় অনুসারে ও-গ্রন্থের ব্যাখ্যা করেন। যিনি জ্ঞানমার্গের পথিক তিনি গীতাকে জ্ঞানপ্রধান ও যিনি ভক্তিমার্গের পথিক তিনি গীতাকে ভক্তিপ্রধান শাস্ত্র হিসাবেই আবহমান কাল ব্যাখ্যা করে এসেছেন। মহাত্মা তিলক তাঁর ভাষ্যে উক্ত কাব্য অথবা স্মৃতির পঞ্চদশখানি পূর্ব-টীকার যুগপৎ বিচার ও খণ্ডন করেছেন। উক্ত পনেরোখানিই যে স্ব স্ব সম্প্রদায় অনুসারেই রচিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মহাত্মা তিলকও স্বসম্প্রদায় অনুসারেই তার নূতন ব্যাখ্যা করেছেন। যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, মহাত্মা তিলক কোন্ সম্প্রদায়ের লোক? তার উত্তর, এ যুগে আমরা সকলেই যে সম্প্রদায়ের লোক, তিনিও সেই একই সম্প্রদায়ের লোক। এ যুগ জ্ঞানের যুগ নয়, বিজ্ঞানের যুগ; ভক্তির যুগ নয়, কর্মের যুগ। মার্কণ্ডেয় পুরাণের মতে, আমাদের জন্মভূমি হচ্ছে কর্মভূমি। ভারতবর্ষ পৌরাণিক যুগে মানুষের কর্মভূমি ছিল কি না জানি না, কিন্তু ভারতবর্ষের এ যুগ যে ঘোরতর কর্মযুগ, সে বিষয়ে, আশা করি, শিক্ষিত সমাজে দ্বিমত নেই। এতদ্দেশীয় ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোক সকলেই, জীবনে না হোক মনে, doctrine of action এর অতি ভক্ত। সন্ন্যাসী হবার লোভ আমাদের কারো নেই; যদি কারো থাকে তো সে একমাত্র পলিটিকাল সন্ন্যাসী হবার। বলা বাহুল্য যে, পলিটিক্স কর্মকাণ্ডের ব্যাপার, জ্ঞানকাণ্ডের নয়, ভক্তিকাণ্ডেরও নয়। সংসারের প্রতি বিরক্তি নয়, আত্যন্তিক অনুরক্তিই পলিটিক্সের মূল। ইউরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রধান প্রভেদ এই কি নয় যে, সে দেশের লোক ‘অজরামরবৎ’ বিদ্যা ও অর্থের চর্চা করে, আর আমরা ‘গৃহীত ইব কেশেষ মৃত্যুনা’ ধর্মচিন্তা করি। আমার কথা যে সত্য তার টাটকা প্রমাণ, মহাত্মা তিলকের একটি আজীবন পলিটিকাল সহকর্মী লালা লাজপৎ রায় এই সেদিন সকলকে বলে গেলেন যে হিন্দুধর্ম আসলে সন্ন্যাসের ধর্ম নয়, কর্মের ধর্ম; এবং সেইসঙ্গে আমাদের সকলকে কায়মনোবাক্যে কর্মে প্রবৃত্ত করবার জন্য গীতার মাত্র দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করবার আদেশ দিয়ে গেলেন, বোধ হয় এই ভয়ে যে, মনোযোগ সহকারে অষ্টাদশ অধ্যায় গীতা পাঠ করলে আমাদের কর্মপ্রবৃত্তি হয়তো নিস্তেজ হয়ে পড়তে পারে। এ ভয় অমূলক নয়।
৩
ইংরেজের শিষ্য আমরা যেমন কর্মের উপাসক, শ্রীধরের শিষ্য নীলকণ্ঠও তেমনি ভক্তির উপাসক ছিলেন, তথাপি তিনিও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে—
ভারতে সর্ববেদার্থো ভারতার্থশ্চ কৃৎস্নশঃ।
গীতায়ামস্তি তেনেয়ং সর্বশাস্ত্রময়ী মতা ॥
কর্মোপাস্তিজ্ঞানভেদৈঃ শাস্ত্রং কাণ্ডত্রয়াত্মকম্।
অন্যে তৃপাসনাকাণ্ডাতৃতীয়ো নাতিরিচ্যতে ॥
তদেব ব্রহ্ম বিদ্ধি ত্বং নেদং যত্তদুপাসতে।
ইতি শ্রুত্যৈব বেদ্যস্য হাপাস্যাদন্যতেরিতা ॥
ইয়মষ্টাদশাধ্যায়ী ক্রমাৎ ষটত্রিকেণ হি।
কর্মোপাস্তিজ্ঞানকাণ্ডত্রিতয়াত্মা নিগদ্যতে ॥
নীলকণ্ঠের এই সরল কথাই হচ্ছে সত্যকথা। গীতার প্রথম ছয় অধ্যায় যে কর্মকাণ্ডের, মধ্যের ছয় অধ্যায় যে ভক্তিকাণ্ডের, আর শেষ ছয় অধ্যায় যে জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত, এরকম তিন অংশে সমান ও পরিপাটি ভাগবাটোয়ারার হিসেব আমরা না মানলেও, এ কথা সকলেই মানতে বাধ্য যে, ও- শাস্ত্রে জ্ঞান কর্ম ও ভক্তি তিনই আছে। ও-গ্রন্থ একে তিন, কিন্তু তিনে এক নয়। গীতায় ও ত্রিকাণ্ডের রাসায়নিক যোগের ফলে কোনো একটি নবকাণ্ডের সৃষ্টি হয় নি। এই কারণে গীতার এমন কোনো এক ব্যাখ্যা হতে পারে না, যা চূড়ান্ত হিসেবে সর্বলোকগ্রাহ্য হবে। কেননা এ ক্ষেত্রে তিনরকম ব্যাখ্যারই সমান অবসর আছে। গীতার অন্তরে নানারূপ ধাতু আছে। কোনো ভাষ্যকারই তাকে ব্যাখ্যার বলে তাঁর মনোমত এক ধাতুতে পরিণত করতে কৃতকার্য হবেন না—তা সে ধাতু জ্ঞানের স্বর্ণই হোক আর কর্মের লৌহই হোক। পূর্বাচার্যেরা প্রধানত গীতাভাষ্যে জ্ঞানভক্তিমার্গই অবলম্বন করেছিলেন; গীতার ধর্ম যে মুখ্যত সন্ন্যাসের ধর্ম নয়, ভগবদ্গীতা যে অবধূতগীতা ও অষ্টাবক্রগীতার জ্যেষ্ঠ সহোদর নয়, এ কথা কিন্তু আজ আমরা জোর করে বলতে পারি।
গীতার মতকে কর্মযোগ বলবার আমাদের অবাধ অধিকার আছে। আর যুগ-ধর্মানুসারে আমরা গীতা নিংড়ে সেই মতই বার করবার চেষ্টা করব। আর, এ প্রযত্ন মহাত্মা তিলকের তুল্য আর কে করতে পারেন? এ যুগের তিনিই যে হচ্ছেন অদ্বিতীয় কর্মযোগী, এ সত্য আর শিক্ষিত অশিক্ষিত কোন্ ভারতবাসীর নিকট অবিদিত? এই গীতাভাষ্যও মহাত্মা তিলকের কর্মযোগের অদ্ভুত ক্রিয়া। জ্ঞানের তরফ থেকে শংকরের ভাষ্য যেমন একমেবাদ্বিতীয়ম্, কর্মের তরফ থেকে মহাত্মা তিলকের ভাষ্যও, আমার বিশ্বাস, তেমনি একমেবাদ্বিতীয়ম্ হয়ে থাকবে।
৪
গীতা কর্মমার্গের জ্ঞানমার্গের কি ভক্তিমার্গের শাস্ত্র, এ তর্ক হচ্ছে এ দেশের ও সেকালের। কিন্তু এই গ্রন্থ নিয়ে এ যুগে এক নূতন তর্কের সৃষ্টি হয়েছে। সে তর্কটা যে কি তা মহাত্মা তিলকের ভাষাতেই বিবৃত করছি—
গ্রন্থ কোথায় রচিত হইয়াছে, কে রচনা করিয়াছে, তাহার ভাষা কিরূপ—কাব্যদৃষ্টিতে তাহাতে কতটা মাধুর্য ও প্রসাদগুণ আছে, গ্রন্থের শব্দরচনা ব্যাকরণশুদ্ধ অথবা তাহাতে কতকগুলি আর্যপ্রয়োগ আছে, তাহাতে কোন্ কোন্ মতের স্থলের কিম্বা ব্যক্তির উল্লেখ আছে, এই-সকল ধরিয়া গ্রন্থের কাল নির্ণয় করা যাইতে পারে কি না…
এরূপ আলোচনাকে মহাত্মা তিলক ‘বহিরঙ্গ পর্যালোচনা’ বলেন। এ আলোচনা আমরা অবশ্য বিলেত থেকে আমদানি করেছি।
পরন্তু, এক্ষণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অনুকরণে এ দেশের আধুনিক বিদ্বানেরা গীতার বাহ্যাঙ্গেরই বিশেষ অনুশীলন করিতেছেন।
এরূপ আলোচনার প্রতি যাঁরা আসক্ত তাঁদের প্রতি মহাত্মা তিলক যে আসক্ত নন, তার পরিচয় তিনি নিজ মুখেই দিয়েছেন। তিনি বলেন,
বাগদেবীর রহস্যজ্ঞ ও তাহার বহিরঙ্গ-সেবক, এই উভয়ের ভেদ দর্শন করিয়া মুরারি কবি এক সরস দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—
অর্ধ্বির্লিঙ্ঘিত এব বানরভটৈঃ কিং ত্বস্য গম্ভীরতাম্।
আপাতালনিমগ্নপীবরতনুজানাতি মন্থাচলঃ।।
আর গ্রন্থরহস্য মধ্যে মন্দার পর্বতের মতো আপাতাল-নিমজ্জিত হওয়ারই নাম অন্তরঙ্গ পর্যালোচনা। মুরারি কবির এই সরস উক্তিটি অবশ্য দেশী বিলেতি বহিরঙ্গ-সেবকদের কর্ণে একটু বিরস ঠেকবে। কিন্তু এ বিষয়ে যাঁরা মদমত্ত জর্মান পাণ্ডিত্যের উল্লম্ফন নিরীক্ষণ করেছেন, তাঁদের পক্ষে মুরারি কবির উক্তির পুনরুক্তি করবার লোভ সংবরণ করা কঠিন।
কাব্যের অন্তরঙ্গের সাধনা ও বহিরঙ্গের সেবা এ দুটি ক্রিয়ার ভিতর যে শুধু প্রভেদ আছে তাই নয়, এর একটি প্রযত্ন অপরটির অন্তরায়। কাব্যের ভিতর থেকে ইতিহাস উদ্ধার করতে বসলে দেখা যায় যে, তার কাব্যরস শুকিয়ে এসেছে আর তার ভিতর নিমজ্জিত ঐতিহাসিক উপলখণ্ড সব দন্তবিকাশ করে হেসে উঠেছে। আমাদের মতো কাব্যরসিকরা কাব্যের সমগ্র রূপ দেখেই মোহিত হই, অপরপক্ষে পণ্ডিতরা কাব্যের রস জিনিসটিকে উপেক্ষা করেন, অন্তত জর্মান পণ্ডিতরা কাব্যের সম্মুখীন হবামাত্র তাকে সম্বোধন করে বলেন,
মাইরি রস ঘুরে বোস্,
দাঁত দেখি তোর বয়েস কতো।
এরই নাম স্কলারশিপ
তবে এরকম ঐতিহাসিক কৌতূহল যখন মানুষের মনে একবার জেগেছে, তখন কাব্যের ঐ বহিরঙ্গ পর্যালোচনায় যোগ দেবার প্রবৃত্তি দমন করা অসম্ভব, বিশেষত আধুনিক বিদ্বান ব্যক্তিদের পক্ষে। অন্যে পরে কা কথা, মহাত্মা তিলকও গীতার বহিরঙ্গ পর্যালোচনার মায়া কাটাতে পারেন নি। তিনি তাঁর গীতাভাষ্যের পরিশিষ্টে অতি বিস্তৃত ভাবেই এই বাহ্যবিচার করেছেন। এতে আমি মোটেই আশ্চর্য হই নি। এই পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে শাস্ত্রবিচারের এ দেশে রাজা ছিলেন স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর। আর মহাত্মা তিলক যে-পুরীকে পুণ্যপুনাপুর বলেন, সেই পুরীই হচ্ছে রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের রাজধানী এবং সেই পুরীতেই এ দেশের যত বড়ো বড়ো ওরিয়েন্টালিস্ট অবতীর্ণ হয়েছেন। কর্মযোগে যত-সব ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের উল্লেখ আছে সে-সবই মহারাষ্ট্রীয়, একটিও বঙ্গদেশীয় নয়। স্বয়ং মহাত্মা তিলক হচ্ছেন এই বিলেতি-দস্তুর-পণ্ডিতদের মধ্যে অগ্রগণ্য। এ বিষয়ে তাঁর কৃতিত্ব এতই অসামান্য যে, পাশ্চাত্য ওরিয়েন্টালিস্ট সমাজেও তিনি অতি উচ্চ আসন লাভ করেছেন।
পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা বিশেষ করে এই মহা প্রশ্ন তুলেছেন যে, মহাভারতে ভগবদ্গীতা প্রক্ষিপ্ত কি না। মহাত্মা তিলক এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে—
যে ব্যক্তি বর্তমান মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন তিনিই বর্তমান গীতাও বিবৃত করিয়াছেন।
এ সিদ্ধান্তে তিনি অবশ্য উপনীত হয়েছেন বাহ্যপ্রমাণের বলে। কেননা তিনি এ কথা স্পষ্ট করে বলেছেন যে—
যাঁহারা বাহ্যপ্রমাণকে মানেন না এবং নিজেরই সংশয়পিশাচকে অগ্রস্থান দেন, তাঁহাদের বিচারপদ্ধতি নিতান্ত অশাস্ত্রীয় সুতরাং অগ্রাহ্য।
মহাত্মা তিলকের মতে,
গীতাগ্রন্থ ব্রহ্মজ্ঞানমূলক, এই ধারণা হইতেই এই সন্দেহ তো প্রথমে বাহির হয়।
আমি অবশ্য আচার্যের শিষ্য নই অর্থাৎ শংকরপন্থী বৈদান্তিক নই, এমন-কি, শংকরকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলতেও আমার তিলমাত্র দ্বিধা নেই। তবুও মহাত্মা তিলকের সংগৃহীত বাহ্যপ্রমাণ আমার মনের সন্দেহ-পিশাচকে একেবারে বধ করতে পারে নি। এর প্রকৃত কারণ তিনিই উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, সন্দেহ নিরঙ্কুশ। আমি অবিদ্বান্, কিন্তু ‘এতদ্দেশীয়’ ও আধুনিক। অতএব আমার মনেও অনেক বিষয়ে সন্দেহ আছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। মনোজগতে ‘আধুনিক ও ‘সংশয়গ্রস্ত’ এ দুটি কথা পর্যায়শব্দ। যাঁর মনে কোনোরূপ সংশয় নেই তাঁর একালে জন্ম আসলে অকালে জন্ম; কারণ দেহে তিনি একেলে হলেও, মনে সেকেলে। এ প্রবন্ধে আমার সেই সন্দেহই আমি ব্যক্ত করতে চাই। পণ্ডিতের বিচারে অবশ্য যোগদান করবার অধিকার আমার নেই, কেননা পণ্ডিত ব্যক্তিদের প্রস্থানভূমি ‘সন্দেহ’ হলেও নিঃসন্দিগ্ধ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তই হচ্ছে তাঁদের গম্যস্থান। আর তাঁরা অবলীলাক্রমেই সেখানে পৌঁছে যান। অপরপক্ষে আমি মহাভারতের নানা দেশ পর্যটন করে অবশেষে কোনো মানসিক রাজপুতনায় উপনীত হতে পারি নি। কারণ মহাভারতের ভিতর আমার পর্যটন শুধু ‘ভ্রমণ কারণ’। সুতরাং আমি অপণ্ডিত ও কাব্যরসিক বাঙালি হিসেবেই এ বিষয়ে একটু উচ্চবাচ্য করতে চাই।
৫
আমাদের শাস্ত্র সম্বন্ধে এই ‘প্রক্ষিপ্ত’ কথাটা চল করেছেন ইউরোপীয় পণ্ডিতরা। এর একটি স্পষ্ট কারণ আছে। আঁদ্রে জিদ নামক জনৈক বিখ্যাত ফরাসি সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির উপর একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি আরম্ভেই বলেছেন যে, গীতাঞ্জলির তনুতা দেখেই তিনি পুলকিত হয়েছিলেন। কারণ তাঁর ভয় ছিল যে, যে দেশের মহাকাব্যের শ্লোক-সংখ্যা হচ্ছে শত- সহস্র, সে দেশের গীতিকাব্যের শ্লোক-সংখ্যা হবে অন্তত এক সহস্ৰ। আঁদ্রে জিদ সংস্কৃত জানেন না, যদি জানতেন তো তিনি মহাভারতের গোড়াতেই দেখতে পেতেন যে, লোমহর্ষণ-পুত্র উগ্রশ্রবা বলেছেন যে, বর্তমান মহাভারত হচ্ছে মূল মহাভারতের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ,
বিস্তীর্য্যেতন্মহজ্জ্ঞানমৃষিঃ সংক্ষিপ্য চাব্রবীৎ।
লোমহর্ষণ-পুত্রের এ কথা শুনলে জিদ সাহেবের যে শুধু লোমহর্ষণ হত তাই নয়, তিনি হয়তো মূর্ছিত হয়ে পড়তেন
ইউরোপীয়েরা হোমারের ইলিয়াডের পরিমাণকেই মহাকাব্যের স্ট্যাণ্ডার্ড মাপ ধরে নিয়েছেন। কিন্তু গ্রীস নামক ক্ষুদ্র দেশের পরিমাণের সঙ্গে ভারতবর্ষ নামক মহাদেশের পরিমাণের তুলনা করলেই তাঁরা বুঝতে পারবেন, কেন ইলিয়াডের মাপের সঙ্গে মহাভারতের মাপ মেলে না ও মিলতে পারে না। কিন্তু ভৌগোলিক হিসেব অনুসারেই যে কাব্যের দেহ সংকুচিত ও প্রসারিত হতে হবে, এ কথা তাঁরা মানতে প্রস্তুত নন। তাঁরা বলেন, মানচিত্রের সঙ্গে মন-চিত্রের কোনো কার্যকারণ সম্বন্ধ নেই। অতএব মহাভারত যখন কাব্য, তখন নৈসর্গিক নিয়মে তা এতাদৃশ মহাকায় হতে পারে না। কাব্যের কথা ছেড়ে দিলেও কাব্যরচয়িতা কবির তো দম বলে একটা জিনিস আছে। কোনো কবি এক দমে মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের পাল্লা ছুটতে পারতেন না। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, মহাভারতের মধ্যে অধিকাংশ শ্লোকই প্রক্ষিপ্ত। এর উত্তর হচ্ছে, ইউরোপীয় পণ্ডিতরা ঐ কাব্য-নামেই ভুলেছেন। মহাভারত কাব্য নয়, মহাভারত হচ্ছে একটি এনসাইক্লোপিডিয়া; সুতরাং এক লক্ষ শ্লোকের অর্থাৎ দু লক্ষ ছত্রের বিশ্বকোষকে সংক্ষিপ্ত বললে আঁদ্রে জিদও কোনো আপত্তি করতে পারবেন না। এ গ্রন্থের নাম সংহিতা না হয়ে কাব্য কি করে হল, তার পরিচয় মহাভারতেই আছে। বেদব্যাসের মনে যখন এ গ্রন্থ জন্মগ্রহণ করে, তখন তিনি ব্রহ্মাকে বলেন যে, আমি মনে মনে একখানি কাব্য রচনা করেছি। সে কাব্যে কি কি জিনিস থাকবে, বেদব্যাসের মুখে তার ফর্দ শুনে স্বয়ং ব্রহ্মাও একটু চমকে ওঠেন ও থমকে যান, তার পর তিনি সসম্ভ্রমে বলেন যে, হে বেদব্যাস, তুমি যখন ও-গ্রন্থকে কাব্য বলতে চাও, তখন ওর নাম কাব্যই হবে, কেননা তুমি কখনো মিথ্যা কথা বল না। এর থেকেই দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমান মহাভারতকে কাব্য বলা যায় কি না, সে বিষয়ে স্বয়ং ব্রহ্মারও সন্দেহ ছিল। কিন্তু তিনি যে ও-গ্রন্থকে অবশেষে কাব্য বলতে স্বীকৃত হয়েছিলেন, তার কারণ মহাভারত একাধারে কাব্য আর এনসাইক্লোপিডিয়া; এবং এই দুই বস্তু একই গ্রন্থের অন্তর্ভূত হলেও মিলেমিশে একদম একাকার হয়ে যায় নি, মোটামুটি হিসেবে উভয়েই চিরকাল নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে আসছে। মহাভারতের যে অংশ আমাদের মতো অবিদ্বান্ লোকেরা পড়ে এবং উপভোগ করে সেই অংশ তার কাব্যাংশ; আর যে অংশ বিদ্বান লোকেরা কষ্টভোগ করে পর্যালোচনা করেন, সেই অংশই তার এনসাইক্লোপিডিয়ার অংশ। এ বিষয়ে বোধ হয় অপণ্ডিত মহলে কোনো মতভেদ নেই।
মহাভারতের এই যুগলরূপের প্রহেলিকাই হচ্ছে ইউরোপীয় পাণ্ডিত্যের শান্তিভঙ্গের মূল কারণ। এ হেঁয়ালির যাহোক-একটা হেস্তনেস্ত না করতে পারলে পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁদের পণ্ডিতি মনের শান্তি ফিরে পাবেন না। এর জন্য তাঁরা সকলে মিলে পাণ্ডিত্যের দাবাখেলা খেলতে শুরু করেছেন। এ খেলায় সকলেই সকলকে মাৎ করতে চান। আমি সে খেলার দর্শক হিসেবে দুটি-একটি উপর- চাল দিচ্ছি। সে চাল নেওয়া না-নেওয়া নির্ভর করছে খেলোয়াড়দের উপর। একটু চোখ চেয়ে দেখলেই দেখতে পাবেন যে, পণ্ডিতের দল ভারতবর্ষের অতীতকে প্রায় বেদখল করে নিয়েছে বেদ এখন ফিললজির, ইতিহাস নিউমিস্ম্যাটিক্সের এবং আর্ট আকিঅলজির অন্তর্ভূত হয়ে পড়েছে—অর্থাৎ একাধারে বিজ্ঞানের ও ইংরেজির। এ অবস্থায় মহাভারত যাতে বাংলা সাহিত্যের হাতছাড়া না হয়ে যায়, সে চেষ্টা আমাদের করা আবশ্যক। তার একমাত্র উপায় হচ্ছে বিচারের হট্টগোলে যোগ দেওয়া। হেঁয়ালি সম্বন্ধে বাংলায় একটা কথা আছে যে–
মূর্খেতে বুঝিতে পারে, পণ্ডিতের লাগে ধন্ধ
এই প্রবচনের উপর ভরসা রেখে এ হেঁয়ালির উত্তর দিতে চেষ্টা করছি।
৬
বলা বাহুল্য যে, কাব্য আর এনসাইক্লোপিডিয়া এক বৃত্তের দুটি ফুল নয়। কাব্য মানুষের অন্তর হতে আবির্ভূত হয়, আর এনসাইক্লোপিডিয়া বাহির থেকে সংগৃহীত। সুতরাং এ উভয়েই যে এক স্থানে ও এক ক্ষণে জন্মলাভ করেছে, এ কথা অবিশ্বাস্য। সুতরাং আমাদের ধরে নিতেই হবে যে, এ দুই পৃথক্ বস্তু; গোড়ায় পৃথক্ ছিল, পরে কালবশে জড়িয়ে গিয়েছে। তার পর প্রশ্ন ওঠে এই যে, কাব্যের স্কন্ধে এনসাইক্লোপিডিয়া ভর করেছে, না, এনসাইক্লোপিডিয়ার অন্তরে কাব্য কোনো ফাঁকে ঢুকে গেছে। এখন এ প্রশ্নের উত্তর নির্ভয়ে দেওয়া যেতে পারে। বিশ্ব অবশ্য কাব্যের পূর্বে সৃষ্ট হয়েছে, কিন্তু বিশ্বকোষ কাব্যের অনেক পরে নির্মিত হয়েছে। এ গ্রন্থের কথার বয়স ওর বক্তৃতার বয়সের চাইতে ঢের বেশি; অর্থাৎ ও-গ্রন্থের সার ওর ভারের চাইতে অনেক প্রাচীন। আর ভাগ্যিস ও-সারটুকু তার উপর চাপানো ভারের ভরে মারা যায় নি, তাই ও-কাব্য আজও বজায় আছে। ও-গ্রন্থের কাব্যাংশ অর্থাৎ সারাংশ যদি বিশ্বকোষের চাপে পিষে যেত, তা হলে মহাভারত হত অর্ধেক বৃহৎসংহিতা আর অর্ধেক বৃহৎকথা; অর্থাৎ তা সকলের পাঠ্য হত না, পাঠ্য হত এক দিকে বৃদ্ধের, অপরদিকে বালকের। এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে পণ্ডিতমণ্ডলী প্রায় একমত। তাঁরা নানা শাস্ত্র ঘেঁটে এই সত্য আবিষ্কার করেছেন যে, মূলে এ কাব্যের নাম ছিল ভারত, তার পরে তার নাম হয়েছে মহাভারত। এ সত্য উদ্ধারের জন্য, আমার বিশ্বাস, নানা শাস্ত্র অনুসন্ধান করবার প্রয়োজন ছিল না। বর্তমান মহাভারতেই ও-দুটি নামই পাওয়া যায়। আর ভারত যে মহাভারত হয়ে উঠেছে তার মহত্ত্ব ও গুরুত্বের গুণে, অর্থাৎ তার পরিমাণ ও ওজনের জন্যে, এ কথা আদিপর্বেই লেখা আছে।
অতঃপর দেখা গেল যে, মহাভারতের পূর্বে ভারত নামক একখানি কাব্য ছিল। মহাভারত আছে, কিন্তু ভারত নেই। অতএব এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ভারত গেল কোথায়? সে গ্রন্থ লুপ্ত হয়েছে, না গুপ্ত হয়েছে? এ প্রশ্নের একটা সোজা উত্তর পেলেই আমরা বর্তমান মহাভারতের কোন্ অংশ তার অপরিমিত মহত্ত্ব ও গুরুত্বের কারণ, তা অনুমান করতে পারব। মহাত্মা তিলক এ প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছেন, তা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। তাঁর বক্তব্য এই যে—
সরল শব্দার্থে ‘মহাভারত’ অর্থে ‘বড় ভারত’ হয়।…বর্তমান মহাভারতের আদিপর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, উপাখ্যানসমূহের অতিরিক্ত মহাভারতের শ্লোকসংখ্যা চব্বিশ হাজার, এবং পরে ইহাও লিখিত হইয়াছে যে, প্রথমে উহার নাম ‘জয়’ ছিল। ‘জয়’ শব্দে ভারতীয় যুদ্ধে পাণ্ডবদের জয় বিবতি বলিয়া বিবেচিত হয়; এবং এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে, ইহাই প্রতীত হয় যে, ভারতীয় যুদ্ধের বর্ণনা প্রথমে ‘জয়’ নামক গ্রন্থে করা হইয়াছিল, গরে সেই ঐতিহাসিক গ্রন্থের মধ্যেই অনেক উপাখ্যান সন্নিবেশি ইয়া উহাই ইতিহাস ও ধর্মাধর্মবিচারেরও নির্ণয়কারী এই এক বড় মহাভারতে পরিণত হইয়াছে।
অর্থাৎ জয় ওরফে ভারত-কাব্য লুপ্ত হয় নি, মহাভারতের অন্তরেই তা গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে। তাই যদি হয় তা হলে মহাভারতের মহত্ত্ব ও গুরুত্বের চাপের ভিতর থেকে জয়ের ক্ষুদ্র দেহ উদ্ধার করা অসম্ভব। ভারত যে লুপ্ত হয় নি, এ বিষয়ে আমি মহাত্মা তিলকের মত শিরোধার্য করি, কারণ সে কাব্যের লুপ্ত হবার কোনো কারণ নেই। সেকালে ছাপাখানা ছিল না, সব গ্রন্থই হাতে লিখতে হত, সুতরাং উপযুক্ত লেখকের অভাবে বড়ো ভারতেরই লুপ্ত হবার কথা, ছোটো ভারতের নয়। সেকালে একটানা শত-সহস্র শ্লোক লেখবার লোক যে কতদূর দুষ্প্রাপ্য ছিল তার প্রমাণ, স্বয়ং ব্রহ্মাও বেদব্যাসের মনঃকল্পিত গ্রন্থ লেখবার ভার গণেশের উপর দিয়েছিলেন। দেশে লেখবার মানুষ পাওয়া গেলে আর হিমালয় থেকে লম্বোদর দেবতাকে টেনে আনতে হত না। ভগবান গজাননও যে ইচ্ছাসুখে এই বিরাট গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করতে রাজি হন নি, তার প্রমাণ তিনি লেখা ছেড়ে পালাবার এক ফন্দি বার করেছিলেন। তিনি ব্যাসদেবকে বলেন যে, আমি বৃথা সময় নষ্ট করতে পারব না। আপনি যদি গড়গড় করে শ্লোক আবৃত্তি করে যান, তা হলে আমি ফসফস্ করে লিখে যাব। আর আপনি যদি একবার মুখ বন্ধ করেন তো আমি একেবারে কলম বন্ধ করব। বেদব্যাস কি চালাকি করে হাঁপ ছেড়ে জিরিয়েছিলেন অথচ হেরম্বকে দিয়ে আগাগোড়া মহাভারত লিখিয়ে নিয়েছিলেন, সে কথা তো সবাই জানে। গণেশকে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দেবার জন্য তিনি অষ্টসহস্র অষ্টশত শ্লোক রচনা করেন, যার অর্থ তিনি বুঝতেন আর শুকদেব বুঝতেন, আর সঞ্জয় হয়তো বুঝতেন, হয়তো বুঝতেন না; সেই ৮৮০০ শ্লোক যদি কেউ মহাভারত থেকে বেছে ফেলতে গারেন, তা হলে তিনি আমাদের মহা উপকার করবেন। তবে জর্মান পণ্ডিত ছাড়া এ কাঁটা বাছবার কাজে আর কেউ হাত দেবেন না।
তার পর, বড়ো বই লেখাও যেমন শক্ত, পড়াও তেমনি শক্ত। এমন-কি, সেকালের পণ্ডিত লোকেও বড়ো বই ভালোবাসতেন না। এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জর্মান পণ্ডিতদের মতো হাজার হাজার পাতা বই গেলা এতদ্দেশীয়দের পক্ষে অসম্ভব। এতদ্দেশীয় পণ্ডিতদের বিরাট গ্রন্থ যে ইষ্ট ছিল না সে কথা মহাভারতেই আছে—
ইষ্টং হি বিদুষাং লোকে সমাসব্যাসধারণম্।
সুতরাং লেখার হিসেব থেকে হোক আর পড়ার হিসেব থেকেই হোক, দু হিসেব থেকেই আমরা মানতে বাধ্য যে, ভারত লুপ্ত হয় নি, ও-কাব্য মহাভাবতের অন্তরে সেই ভাবে অবস্থিতি করছে, যে ভাবে শকুন্তলার আংটি মাছের পেটে অবস্থিতি করেছিল।
আমরা যদি মহাভারতের ভিতর থেকে ভারতকে টেনে বার করতে পারি তা হলে ভারতের অন্তরে ও অঙ্গে কোন্ কোন্ উপাখ্যান ইতিহাস দর্শন ও ধর্মাধর্মের বিচার প্রক্ষিপ্ত ও নিক্ষিপ্ত হয়েছে, তার একটা মোটামুটি হিসেব পাই। আর যদি ধরে নিই যে, মহাভারতের অতিরিক্ত মালমসলা সব ঐ ভারত-কাব্যের ভিতর interpolated হয়েছে, তা হলে অবশ্য ঐ শ্লোকস্তূপের ভিতরে ভারতের সন্ধান আমরা পাব না। আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যিনি গ্রীক দেবতা হারকিউলিসের মতো ওরকম পঙ্কোদ্ধার করতে প্রবৃত্ত হবেন। অপরপক্ষে গ্রীক বীর অ্যালেকজাণ্ডারের মতো এই জটিল গ্রন্থের Gordian Knot যদি আমরা দ্বিখণ্ড করতে পারি, তা হলে হয়তো মহাভারত থেকে ভারতকে পৃথক্ করে নিতেও পারি।
৭
ইন্টারপোলেশনের দৌলতেই ভারত যে মহাভারতে পরিণত হয়েছে, সে বিষয়ে দেশী বিলেতি সকল আধুনিক পণ্ডিত একমত।
কিন্তু এই ইন্টারপোলেশন, ভাষান্তরে ‘প্রক্ষিপ্ত’, কথাটা তাঁরা যে কি অর্থে ব্যবহার করেন, সেটা যথেষ্ট স্পষ্ট নয়।
যদি তাঁদের মত এই হয় যে, যেমন মোরগের পেটে চাল পুরে দিয়ে একাধারে কাবাব ও পোলাও বানানো হয়, তেমনি ভারতের অন্তরে নানা বস্তু নানা যুগে পুরে দিয়ে তার গুরুত্ব ও মহত্ত্ব সাধন করা হয়েছে, তা হলে সে মত আমি সন্তুষ্ট মনে গ্রাহ্য করতে পারি নে।
আমার বিশ্বাস, বর্তমান মহাভারতের কতক অংশ ভারতের ভিতর পুরে দেওয়া হয়েছে, এবং অনেক অংশ তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। প্রক্ষিপ্ত অংশের বিচার এখন স্থগিত রেখে যদি আমরা তার সংযোজিত অংশকে ভারতকাব্য থেকে বিযুক্ত করতে পারি, তা হলে আমাদের সমস্যা অনেক সরল হয়ে আসে।
আমরা যদি সাহস করে এক কোপে মহাভারতকে দ্বিখণ্ড করে ফেলতে পারি, তা হলে, আমার বিশ্বাস, ভারতকে মহাভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারি। বর্তমান মহাভারতের নয় পর্ব হচ্ছে প্রাচীন ভারত আর তার বাদবাকি নয় পর্ব হচ্ছে অর্বাচীন মহাভারত—এই হিসেবটাই হচ্ছে গণিতের হিসেবে সোজা; অতএব অপণ্ডিতদের কাছে গ্রাহ্য হওয়া উচিত।
প্রথম নয় পর্বের ভিতর অবশ্য অনেক প্রক্ষিপ্ত বিষয় আছে, যা পূর্বে ভারত-কাব্যের অঙ্গস্বরূপ ছিল না; কিন্তু শেষ নয় পর্বের ভিতর সম্ভবত এমন একটি কথাও নেই, যা পূর্বে ভারতকাব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।
সংক্ষেপে দুইখানি বই একসঙ্গে জুড়ে মহাভারত তৈরি করা হয়েছে। এ দুইখানি গ্রন্থকে পূর্বভারত ও উত্তরভারত আখ্যা দেওয়া ঢলে। সকলেই জানেন যে, সংস্কৃত সাহিত্যে এরকম কাব্য আরো অনেক আছে। কাদম্বরী কুমারসম্ভব মেঘদূত প্রভৃতির এইরকম দুটি স্পষ্ট ভাগ আছে। পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ অবশ্য একই হাতের লেখা এবং একই কাব্যের বিভিন্ন অঙ্গ। কাদম্বরীর পূর্বভাগ বাণভট্টের রচনা, আর উত্তরভাগ তাঁর পুত্রের। কুমারসম্ভবের পূর্বভাগ কালিদাসের রচনা, আর উত্তরভাগ, আর যারই লেখা হোক, কালিদাসের লেখা নয়। এমন-কি রামায়ণের উত্তরকাণ্ড যে বাল্মীকির লেখনীপ্রসূত নয় সে বিষয়েও সন্দেহ নেই।
৮
মহাভারতকে এরকম দ্বিধাবিভক্ত করা নেহাত গোঁয়ারতুমি নয়। সত্যসত্যই দুটি আধখানিকে গ্রথিত করে মহাভারত নামে একখানি গ্রন্থ করা হয়েছে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ চিরকালই রয়ে যাবে, কেননা মহাভারত সংক্রান্ত বড়ো বড়ো আবিষ্কার সম্বন্ধে সমান সন্দেহ রয়ে গেছে। একটি দৃষ্টান্ত দিই। ডালমান Dahlmann নামক জনৈক ধনুর্ধর জর্মান পণ্ডিত আজীবন গবেষণার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মহাভারত খৃস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত হয়েছে। অপর পক্ষে? হোমান Holtzmann নামক অপর-একটি সমান ধনুর্ধর জর্মান পণ্ডিত আজীবন গবেষণার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মহাভারত খৃস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই উভয় আবিষ্কারই যুগপৎ সমান সত্য হতে পারে না। ফলে এর একটিও সত্য কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ লোকের মনে থেকেই যায়। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও জর্মান পণ্ডিতদের প্রতি ভক্তি কারো কমে নি। বিদ্বান্ ব্যক্তিদের পদানুসরণ করেই আমি আমার মত ব্যক্ত করছি। সে মত যাঁর খুশি গ্রাহ্য করতে পারেন, যাঁর খুশি অগ্রাহ্য করতে পারেন; শুধু আমার মতকে সম্পূর্ণ গাঁজাখুরি মনে করবেন না। আমার মত আমি শূন্যে খাড়া করি নি। এ সত্যের মূল মহাভারতের ভিতরেই আছে। আপনাদের পূর্বে বলেছি যে, পুরাকালে ভারত-কাব্যের অপর নাম ছিল জয়-কাব্য; অর্থাৎ এ কাব্যে ছিল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও যুদ্ধজয়ের কথা; সুতরাং যুদ্ধজয়ের পরবর্তী কোনো বিষয়ের বর্ণনা বা আলোচনা এতে ছিল না। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেছেন যে, মহাভারত হচ্ছে যুদ্ধপ্রধান গ্রন্থ, এবং ও-কাব্যের প্রধান বিষয় যা, তা শেষ হয়েছে সৌপ্তিকপর্বে। এ কথা যে সত্য, সে বি আর সন্দেহ নেই। যুদ্ধ করবার লোক না থাকলে আর যুদ্ধ করা যায় না। আর সৌপ্তিকপর্বের শেষে দেখতে পাই যে, অশ্বত্থামা মুমূর্ষু দুর্যোধনকে বলেছেন যে, উভয় পক্ষের সকল যোদ্ধা নিহত হয়েছে; অবশিষ্ট আছে শুধু কৌরব পক্ষের তিনজন—কৃপাচার্য কৃতবর্মা ও স্বয়ং অশ্বত্থামা। অপরপক্ষে পাণ্ডবদের ভিতর অবশিষ্ট আছে সাতজন, পঞ্চপাণ্ডব সাত্যকি ও কৃষ্ণ। এ কথা বলেই অশ্বত্থামা চলে গেলেন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের আশ্রমে, কৃতবর্মা স্বরাষ্ট্রে ও কৃপাচার্য হস্তিনাপুরে। এইখানেই ভারত-নাটকের যবনিকাপতন হয়েছে। এর পর মহাভারতে যা আছে সে হচ্ছে যুদ্ধের নয়, শান্তির কথা। বর্তমান মহাভারত অবশ্য এ দেশের ওঅর অ্যাণ্ড পীস্ নামক মহাকাব্য। কিন্তু মূল ভারত ছিল ইলিঅডের মতো শুধু যুদ্ধকাব্য। কাব্যকে আমরা চল বলি। এ হিসেবে সৌপ্তিকপর্বকেই আমরা ভারত-কাব্যের শেষ পর্ব বলে স্বীকার করতে বাধ্য। আদিপর্বে আছে যে, মহাভারত নামক মহাবৃক্ষের সৌপ্তিকপর্ব হচ্ছে প্রসূন, আর শান্তিপর্ব মহাফল। ফুল যখন ফলে পরিণত হয়, তখনই তা কাব্যের বহির্ভূত হয়ে পড়ে। আমার এ অনুমান যদি সত্য হয়, তা হলে এই উত্তরভারতে কোন শ্লোক প্রক্ষিপ্ত আর কোন শ্লোক নয়, তা নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই, কারণ ও-গ্রন্থ আগাগোড়াই প্রক্ষিপ্ত। প্রক্ষিপ্ত অংশের সন্ধান করতে হবে পূর্বভারতে। এতে এই খোঁজাখুঁজির কাজটা অর্ধেক কম হয়ে আসে কি না?
৯
সৌপ্তিকপর্ব ভারত-কাব্যের অন্তর্ভূত স্বীকার করলে আমার কল্পিত বিভাগ দুটি ঠিক সমান হয় না। কারণ সৌপ্তিকপর্ব হচ্ছে বর্তমান মহাভারতের দশম পর্ব। কিন্তু আসলে আমার হিসেবে ভুল হয় নি। মহাভারতের একটি পর্ব যা পূর্বভাগে স্থান পেয়েছে, তা আসলে উত্তরভাগের জিনিস। আদিপর্ব হচ্ছে মহাভারতের অন্তপর্ব। ও-পর্বের প্রথম অধ্যায় হচ্ছে আমরা যাকে বলি Preface, দ্বিতীয় অধ্যায় Table of Contents এবং তার পরবর্তী কথা-প্রবেশপর্ব হচ্ছে Introduction। এখন এ কথা কে না জানে যে, মুখপত্র সূচি ও ভূমিকা বইয়ের গোড়াতে ছা। হলেও লেখা হয় সবশেষে। আমার মত যে সত্য, তার প্রমাণ ‘আদি’ শব্দের ব্যাখ্যায় নীলকণ্ঠ স্পষ্ট বলেছেন –
আদিত্বঞ্চাস্য ন প্রাথম্যাৎ।
তিনি অবশ্য এর পরে একটা কথা জুড়ে দিয়েছেন, যথা—
কিন্তু সর্বেষামাদিরুৎপত্তিরিহ কীর্ত্যতে ইতি।
কোনো কাব্যের গোড়াতেই কবি কখনো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি কীর্তন করেন না। এই বিশ্বসৃষ্টির বিবরণ ভার -কাব্যের বিষয় নয়, ভারত বিশ্বকোষের অঙ্গ।
মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বকে দুটি সমান ভাগে বিভক্ত করবার আর-একটি মুশকিল আছে। ভারত-কাব্য সৌপ্তিকপর্বে শেষ করলে ও-কাব্যের ভিতর থেকে স্ত্রীপর্ব বাদ পড়ে। কিন্তু ও-পর্বকে ভারতের কাব্যাংশ থেকে আমি কিছুতেই বহিষ্কৃত করতে পারি নে। গান্ধারীর বিলাপ না থাকলে ভারত-কাব্যের অঙ্গহানি হয়। অপর পক্ষে ও-বিলাপকে আমি কিছুতেই উত্তরভারতের অন্তর্ভূত করতে পারি নে। এপিকের সুর যার কানে লেগেছে সে ব্যক্তি কখনোই স্ত্রীপর্বকে এনসাইক্লোপিডিয়ার অঙ্গ বলে স্বীকার করতে পারে না। এর প্রমাণস্বরূপ আমি গান্ধারীর মুখের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। শ্মশানে পরিণত যুদ্ধক্ষেত্রে দুঃখের চরম দশায় উপনীত গান্ধারী যখন শ্রীকৃষ্ণকে বিগতেশ্বর কুরুকুলাঙ্গনাদের একে একে দেখিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন তিনি নিজের কন্যা দুঃশলাকে দেখিয়ে বলেন—
হা হা ধিগ্দুঃশলাং পশ্য বীতশোকভয়ামিব।
শিরোভর্তুরনাসাদ্য ধাবমানামিতস্ততঃ ॥
যাঁরা শান্তিপর্ব ও অনুশাসনপর্ব লিখেছেন, তাঁরা শতসহস্র শ্লোক লিখলেও এর তুল্য একটি শ্লোক লিখতে পারেন না। এর প্রতি কথার ভিতর থেকে মহাকবির হাত ফুটে বেরচ্ছে। ভারত-কাব্যের ভিতর যদি স্ত্রীপর্বকে স্থান দেওয়া যায়, তা হলে সেখান থেকে আর-একটি পর্বকে স্থানচ্যুত করতে হয়। আমি বনপর্বকে পূর্বভারত থেকে বহিষ্কৃত করতে প্রস্তুত আছি। ও-পর্বের যে পনেরো-আনা- তিন-পাই প্রক্ষিপ্ত, এ বিষয়ে সকল পণ্ডিত, মায় তিলক, একমত। সেই এক পাই আমি বিরাটপর্বের অন্তর্ভূত করে, বাদবাকি অংশটি উপাখ্যানপর্ব নামে উত্তরভারতে স্থান দিতে চাই। আর তাতে যদি কারো আপত্তি থাকে তা হলে বলি, পূর্বভারত দশ পর্ব, আর উত্তরভারত অষ্ট পর্ব।
১০
আমি জনৈক বন্ধুর মুখে শুনলুম যে, শান্তিপর্ব থেকে শুরু করে স্বর্গারোহণপর্ব পর্যন্ত অষ্টপর্ব যে মহাভারতের অন্তরে পাইকেরি হিসেবে প্রক্ষিপ্ত, এ কথা নাকি সবাই জানে। যদি তাই হয় তো আমার এ গবেষণার ফল হচ্ছে পণ্ডিতের তেলা মাথায় তেল ঢালা। কিন্তু আমার এই গবেষণা যে বৃথা হয় নি, তার প্রমাণ, মহাত্মা তিলক এ সত্য হয় জানতেন না, নয় মানতেন না। আর পাণ্ডিত্যের হিসেবে তিনি কোনো জর্মান পণ্ডিতের চাইতে কম ছিলেন না। তিনি বলেছেন যে, বর্তমান মহাভারত এক হাতের লেখা। বর্তমান মহাভারত যে এক হাতের লেখা নয়, এবং এক সময়ের লেখা নয়, তাই প্রমাণ করবার জন্য আমি এই অনধিকারচর্চা করতে বাধ্য হয়েছি।
আমার আসল জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, গীতা মহাভারতের ভিতর প্রক্ষিপ্ত কি না। বর্তমান মহাভারতের শেষ আট পর্ব ছেঁটে দিলেও এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না, কেননা গীতা পূর্বভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্ভূত, উত্তরভারতের নয়। সুতরাং যে সমস্যার মীমাংসা করতে হবে সে হচ্ছে এই যে, গীতা ভারত-কাব্যের অঙ্গ, না, তার অঙ্গস্থ পরগাছা? গীতাকাব্যের রূপ দেখেই আমরা ধরে নিতে পারি নে যে, ও ফুল ভারত-কাব্যের অন্তর থেকে ফুটে উঠেছে। অর্কিডের ফুলও চমৎকার, কিন্তু তার মূল ঝোলে আকাশে।
উক্ত বিচার আমার সময়ান্তরে করবার ইচ্ছা আছে। এ স্থলে শুধু একটা কথা বলে রাখি আদিপর্বে ভীষ্মপর্বকে বিচিত্রপূর্ব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এ পর্বের এই বৈচিত্র্যের কারণ, এতে যুদ্ধপ্রসঙ্গ ব্যতীত হরেকরকমের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ আছে। ভীষ্মপর্ব এক হাতের লেখা নয়। এ-সব প্রসঙ্গের বেশির ভাগই প্রক্ষিপ্ত এবং গীতাও তাই কি না, সেইটিই বিচার্য।
কার্তিক ১৩৩৪