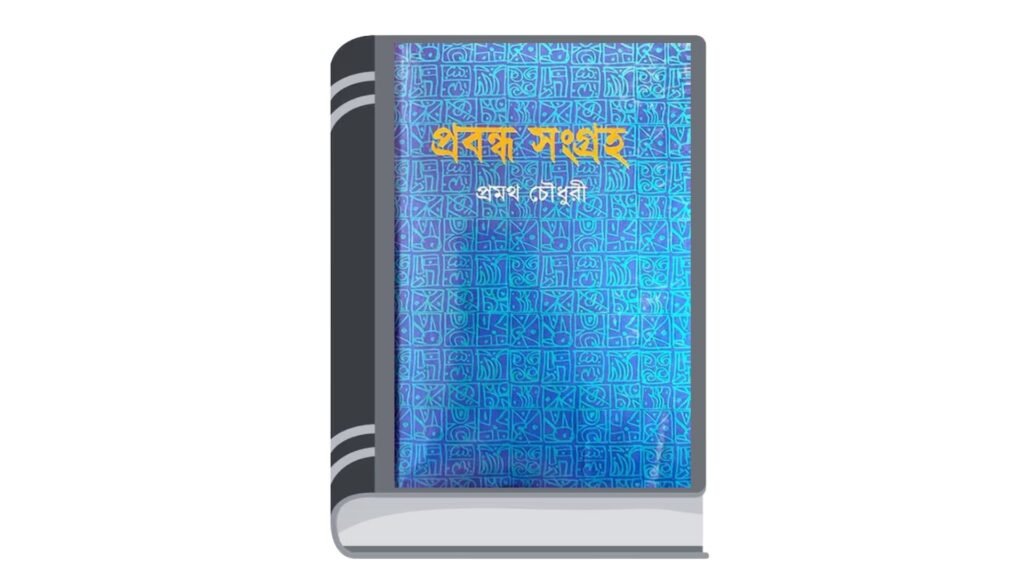নূতন ও পুরাতন
নূতন ও পুরাতন
আমাদের সমাজে নূতন-পুরাতনের বিরোধটা সম্প্রতি যে বিশেষ টনটনে হয়ে উঠেছে, এরূপ ধারণা আমার নয়। আমার বিশ্বাস, জীবনে আমরা সকলেই একপথের পথিক, এবং সে পথ হচ্ছে নতুন পথ। আমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রভেদ এই যে, কেউ-বা পুরাতনের কাছ থেকে বেশি সরে এসেছি, কেউ-বা কম। আমাদের মধ্যে আসল বিরোধ হচ্ছে মত নিয়ে। মনোজগতে আমরা নানা পন্থী। আমাদের মুখের কথায় ও কাজে যে সব সময়ে মিল থাকে, তাও নয়।
এমন-কি, অনেক সময়ে দেখা যায় যে যাদের সামাজিক ব্যবহারে সম্পূর্ণ ঐক্য আছে, তাদের মধ্যেও সামাজিক মতামতে সম্পূর্ণ অনৈক্য থাকে, অন্তত মুখে। সুতরাং নূতন-পুরাতনে যদি কোথায়ও বিবাদ থাকে তো সে সাহিত্যে, সমাজে নয়।
এ বাদানুবাদ ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে, তাই শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল এই পরম্পরবিরোধী মতদ্বয়ের সামঞ্জস্য করে দিতে উদ্যত হয়েছেন।(১) তিনি নূতন ও পুরাতনের মধ্যে একটি মধ্যপথ আবিষ্কার করেছেন, যেটি অবলম্বন করলে নূতন ও পুরাতন হাত-ধরাধরি করে উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে পারবে-যে পথে দাঁড়ালে নতুন ও পুরাতন পরস্পরের পাণিগ্রহণ করতে বাধ্য হবে এবং উভয়ে মনের মিলে সুখে থাকবে; সে পথের পরিচয় নেওয়াটা অবশ্য নিতান্ত আবশ্যক। যারা এ পথও জানে, ও পথও জানে কিন্তু দুঃখের বিষয় মরে আছে, তারা হয়তো একটা নিষ্কণ্টক মধ্যপথ পেলে বেঁচে উঠবে।
.
২.
ঘটকালি করতে হলে ইনিয়ে-বিনিয়ে-বানিয়ে নানা কথা বলাই হচ্ছে মামুলি দস্তুর। সুতরাং নূতনের সঙ্গে পুরাতনের সম্বন্ধ করতে গিয়ে বিপিনবাবুও নানা কথার অবতারণা করতে বাধ্য হয়েছেন। তার অনেক ছোটোখাটো কথা সত্য, আর কতক বড়ো বড়ো কথা নতুন। তবে তাঁর কথার ভিতর যা সত্য তা নতুন নয়, আর যা নতুন তা সত্য কি না তা পরীক্ষা করে দেখা আবশ্যক।
বিপিনবাবু প্রথমে আমাদের সমাজে নূতন ও পুরাতনের বিরোধের কারণ নির্ণয় করে পরে তার সময়ের উপায়-নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে আমরা ইংরাজি শিখিয়া, য়ুরোপের সভ্যতা ও সাধনার বাহিরটা দেখিয়া…ঘর ছাড়িয়া বাহিরের দিকে ছুটিয়াছিলাম।
এই ছোটাটাই হচ্ছে নূতন এবং পুরাতনের সঙ্গে বিচ্ছেদের এইখানেই সূত্ৰপাত। আবার আমরা ঘরে ফিরে এসেছি। অতএব এখন মিলনের কাল উপস্থিত হয়েছে। গত-শতাব্দীতে দেশসুদ্ধ লোকের মন যে এক-লক্ষ্যে সমুদ্র লঙ্ঘন করে বিলাতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল এবং এ শতাব্দীতে সে মন যে আবার উলটো লাফে দেশে ফিরে এসেছে, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। আমাদের মনের দিক থেকে দেখতে গেলে উনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীতে যে বিশেষ কোনো প্রভেদ আছে তা নয়, যদি থাকে তো সে উনিশ-বিশ। আজকালকার দিনে ইউরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব ঢের বেশি লোকের মনে ঢের বেশি পরিমাণে স্থান লাভ করেছে। বরং এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, বহু, ইউরোপীয় মনোভাব দেশের মনে এত বসে গেছে যে, সে ভাব দেশী কি বিদেশী তাও আমরা ঠাওর করতে পারি নে। উদাহরণস্বরূপে দেখানো যেতে পারে যে, একটি বিশেষজাতীয় মনোভাব, যার ক থেকে ক্ষ পর্যন্ত প্রতি অক্ষর বিদেশী, তাকে আমরা বলি স্বদেশী।
ইউরোপীয় সভ্যতার বাইরের দিকটা দেখে অবশ্য জনকতক সেদিকে ছুটেছিলেন, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা অতি সামান্য এবং তাঁদের ঘরে ফিরে না আসাতে দেশের কোনো ক্ষতি নেই, বরং তাঁদের ফেরাতে বিপদ আছে। বিপিনবাবু বলেন–
একদিন আমরা বেড়া ভাগিয়া ঘর ছাড়িয়া পলাইয়াছিলাম, আজ বাড়ি খাইয়া, ফিরিয়া আসিয়াছি। সত্য কথাটা তাহা নয়।
কিন্তু এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। আমাদের মধ্যে যারা ইউরোপের সভ্যতার বাহ্যচাকচিক্যে অন্ধ হয়ে বেড়া ভেঙে ছুটেছিল তারাই আবার বাড়ি খেয়ে বাড়ি ফিরেছে। পাঁচনই তাদের পক্ষে জ্ঞানাঞ্জনশলাকার কাজ করেছে। কেননা, ও-জাতির অন্ধতা সারাবার সংগত বিধান এই—‘নেত্ররোগে সমুৎপন্নে কর্ণং ছিত্ত্বা’ দেগে দেওয়া।
বিপিনবাবু বলেন–
কেহ কেহ মনে করেন, একদিন যেমন আমরা স্বদেশের যাহা-কিছু, তাহাকেই হীনচক্ষে দেখিতাম, আজ বুঝি সেইরূপ বিচারবিবেচনা-বিরহিত হইয়াই, স্বদেশের যাহা-কিছু, তাহাকেই ভাল বলিয়া ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছি।
বিপিনবাবুর মতে এরূপ মনে করা ভুল। কিন্তু এরূপ শ্রেণীর লোক আমাদের সমাজে যে মোটেই বিরল নয়, সে কথা নারায়ণ(২) পত্রে ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল স্পষ্টাক্ষরে লিখে দিয়েছেন। তাঁর মতে—
য়ুরোপের জনসাধারণে যেমন আপনাদের অসাধারণ অভ্যুদয় দেখিয়া, য়ুরোপের বাহিরে যে প্রকৃত মানুষ বা শ্রেষ্ঠতর সভ্যতা আছে বা ছিল বলিয়া ভাবিতে পারে না; আমাদের এই অভ্যুদয় নাই বলিয়াই যেন আরও বেশী করিয়া কিয়ৎপরিমাণে এই প্রত্যক্ষ হীনতার অপমান ও বেদনার উপশম করিবার জন্যই, সেইরূপ আমরাও নিজেদের সনাতন সভ্যতা ও সাধনার অত্যধিক গৌরব করিয়া, জগতের অপরাপর সভ্যতা ও সাধনাকে হীনতর বলিয়া ভাবিয়া থাকি।
ডাক্তার শীল বলেন—
[এরূপ বিচার] স্বজাতিপক্ষপাতিত্ব-দোষে দুষ্ট, [অতএব] সত্যভ্রষ্ট।
আমাদের পক্ষে এরূপ মনোভাবের প্রশ্রয় দেওয়াতে যে সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করা হয়, সে বিষয়ে তিলমাত্রও সন্দেহ নেই। কেননা, ইউরোপের জনসাধারণের জাতীয় অহংকার জাতীয় অভ্যুদয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত; আমাদের জাতীয় অহংকার জাতীয় হীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত; ইউরোপের অহংকার তার কৃতিত্বের সহায়, আমাদের অহংকার আমাদের অকর্মণ্যতার পষ্ঠপোষক। সুতরাং এ শ্রেণীর লোকের বারা নতুন ও পুরাতনের বিরোধের যে সমবয় হবে, এরূপ আশা করা বাধ্য। যাঁরা মদ ছেড়ে আফিং ধরেন তাঁরা যদি কোনো-কিছুর সমন্বয় করতে পারেন তো সে হচ্ছে এই দুই নেশার। মদ আর আফিং এই দুটি জড়িতে চালাতে পারে সমাজে এমন লোকের অভাব নেই।
আসল কথা, নবশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে হাজারে নশো নিরানব্বই জন কস্মিনকালে প্রাচীন সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন নি। অদ্যাবধি তাঁরা কেবলমাত্র অশনে বসনে ব্যসনে ও ফ্যাশনে সামাজিক নিয়ম অতিক্রম করে আসছেন; কেননা, এ-সকল নিয়ম লঘন করবার দরুন তাঁদের কোনোরূপ সামাজিক শাস্তিভোগ করতে হয় না। পুরাতন সমাজধর্মের অবিরোধে নূতনকামের সেবা করাতে সমাজ কোনোরূপ বাধা দেয় না, কাজেই শিক্ষিত লোকেরা ঘরে ঘরে নিজের চরকায় বিলেতি তেল দেওয়াটাই তাঁদের জীবনের ব্রত করে তুলেছেন। এ শ্রেণীর লোকেরা দায়ে পড়ে সমাজের যে-সকল পরোনো নিয়ম মেনে চলেন, অপরের গায়ে পড়ে তারই নতুন ব্যাখ্যা দেন। এরা নতুন-পুরাতনের বিরোধভঞ্জন করেন নি; যদি কোনোকিছুর সমন্বয় করে থাকেন তো সে হচ্ছে সামাজিক সুবিধার সঙ্গে ব্যক্তিগত আরামের সময়।
পুরাতনের সঙ্গে নূতনের বিরোধের সৃষ্টি সেই দু-দশ জনে করেছেন, যাঁরা সমাজের মরচে-ধরা চরকায় কোনোরূপ তৈল প্রদান করবার চেষ্টা করেছেন—সে তেল দেশীই হোক, আর বিদেশীই হোক। এর প্রমাণ রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দয়ানন্দ স্বামী, কেশবচন্দ্র সেন ইত্যাদি। এর প্রথম তিনজন সমাজের দেহে যে স্নেহ প্রয়োগ করেছিলেন, সেটি খাঁটি দেশী এবং সংস্কৃত। অথচ এরা সকলেই সমাজদ্রোহী বলে গণ্য।
সমাজসংস্কার, অর্থাৎ পুরাতনকে নূতন করে তোলবার চেষ্টাতেই এ দেশে নন-পতনে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে।
বিপিনবাবুর মুখের কথায় যদি এই বিরোধের সময় হয়ে যায়, তা হলে আমরা সকলেই আশীর্বাদ করব, যে তার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।
.
৩.
দুটি পরস্পরবিরোধী পক্ষের মধ্যস্থতা করতে হলে নিরপেক্ষ হওয়া দরকার, অথচ একপক্ষ-না-একপক্ষের প্রতি টান থাকা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। বিপিনবাবুও এই সহজ মানবধর্ম অতিক্রম করতে পারেন নি। তার নানান উলটাপালটা কথার ভিতর থেকে তাঁর নূতনের বিরুদ্ধে নন ঝাঁজ ও পুরাতনের প্রতি নূতন ঝোঁক ঠেলে বেরিয়ে পড়েছে। উদাহরণস্বরূপ তাঁর একটি কথার উল্লেখ করছি।
সকলেই জানেন যে, পুরাতন সংস্কারের নাম শুনতে পারে না; কারণ সুপ্তকে জাগ্রত করবার জন্য নূতনকে পতনের গায়ে হাত দিতে হয়–তাও আবার মোলায়েমভাবে নয়, কড়াভারে। বিপিনবাবু তাই সংস্কারকের উপর গায়ের বা ঝেড়ে নিজেকে ধরা দিয়েছেন। এর থেকেই বোঝা যায় যে, পালমহাশয়, যারা সমাজকে বদল করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে, আর যারা সমাজ অটল করতে চায় তাদের পক্ষে।
বিপিনবাবু বলেন–
দুনিয়াটা সংস্কারকের সৃষ্টিও নয়, আর সংস্কারকের হাত পাকাইবার জন্য সৃষ্টও হয় নাই।
দুনিয়াটা বে কি কারণে সৃষ্টি করা হয়েছে তা আমরা জানি নে, তার কারণ সৃষ্টিকর্তা আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করে ও-কাজ করেন নি। তবে তিনি যে পাল মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে সৃষ্টি করেছেন, এমনও তো মনে হয় না। কারণ, দুনিয়া আর যে জন্যই সৃষ্ট হোক, বক্তৃতাকারের গলা-সাধবার জন্য হয় নি। সৃষ্টির পূর্বের খবর আমরাও জানি নে, বিপিনবাবুও জানেন না; কিন্তু জগতের সঙ্গে মানুষের কি সম্পর্ক তা আমরা সকলেই অল্পবিস্তর জানি। ম্লেচ্ছ ভাষায় যাকে দুনিয়া বলে, হিন্দুদর্শনের ভাষায় তার নাম ‘ইদং’। ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল নারায়ণ পত্রে সেই ইদংএর নিম্নলিখিত পরিচয় দিয়েছেন–
ইদংকে যে জানে, যে ইদংএর জ্ঞাতা ও ভোক্তা, আপনার কর্মের দ্বারা যে ইদংকে পরিচালিত ও পরিবর্তিত করিতে পারে বলিয়া, যাহাকে এই ইদংএর সম্পর্কে কৰ্ত্তাও বলা যায়—সেই মানুষ অহং পদবাচ্য।
অর্থাৎ মানুষ দুনিয়ার জ্ঞাতা ও কর্তা। শুধু তাই নয়, মানুষ ইদংএর কতা বলেই তার জ্ঞাতা। মনোবিজ্ঞানের মূল সত্য এই যে, বহির্জগতের সঙ্গে মানুষের যদি ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার কারবার না থাকত তা হলে তার কোনোরূপ জ্ঞান আমাদের মনে জন্মাত না। মানুষের সঙ্গে দুনিয়ার মূলসম্পর্ক ক্রিয়াকর্ম নিয়ে। আমাদের ক্রিয়ার বিষয় না হলে দুনিয়া আমাদের জ্ঞানের বিষয়ও হত না, অর্থাৎ তার কোনো অস্তিত্ব থাকত না। এবং সে ক্রিয়াফল হচ্ছে ইদংএর পরিচালন ও পরিবর্তন, আজকালকার ভাষায় যাকে বলে সংস্কার। সৃষ্টির গূঢ়তত্ত্ব না জানলেও মানুষে এ কথা জানে যে, তার জীবনের নিত্য কাজ হচ্ছে সৃষ্টপদার্থের সংস্কার করা। মানুষ যখন লাঙলের সাহায্যে ঘাস তুলে ফেলে ধান বোনে তখন সে পৃথিবীর সংস্কার করে। মানুষের জীবনে এক কৃষি ব্যতীত অপর কোনো কাজ নেই। এই দুনিয়ার জমিতে সোনা ফলাবার চেষ্টাতেই মানুষ তার মনুষ্যত্বের পরিচয় দেয়। ঋষির কাজও কৃষিকাজ, শুধু সে কৃষির ক্ষেত্র ইদং নয় অহং। সুতরাং সংস্কারকদের উপর বক্র দৃষ্টিপাত করে বিপিনবাবু দৃষ্টির পরিচয় দেন নি, পরিচয় দিয়েছেন শুধু বক্রতার।
শাস্ত্রে বলে যে, ক্রিয়াফল চারপ্রকার–উৎপত্তি প্রাপ্তি বিকার ও সংস্কার। কি ধর্ম কি সমাজ, কি রাজ্য, যার সংস্কারে হাত দেন তারই বিকার ঘটান, এমন লোকের অভাব যে বাংলায় নেই, সম্প্রতি তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। একই উপাদান নিয়ে কেউ গড়েন শিব, কেউ-বা বাঁদর। এ অবশ্য মহা আক্ষেপের বিষয়; কিন্তু তার থেকে এ প্রমাণ হয় না যে, দেশসুদ্ধ লোকের মাটির সুমুখে হাতজোড় করে বসে থাকতে হবে।
.
৪.
বিপিনবার মতে নূতনে-পুরাতনে মিলনের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে নূতন; কারণ নূতনই হচ্ছে মূল বিবাদী। সুতরাং নূতনকে বাগ মানাতে হলে তাকে কিঞ্চিৎ আক্কেল দেওয়া দরকার।
নূতন তার গোঁ ছাড়তে চায় না, কেননা সে চায় উন্নতি। কিন্তু সে ভুলে যায় যে, জাগতিক নিয়মানুসারে উন্নতির পথ সিধে নয়, প্যাঁচালো। উন্নতি যে পদেপদে অবনতিসাপেক্ষ তার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে। বিপিনবাবু এই বৈজ্ঞানিক সত্যটির বক্ষ্যমাণ রূপ ব্যাখ্যা করেছেন–
তালগাছের মতন মানুষের মন বা মানবসমাজ একটা সরলরেখার ন্যায় ঊর্ধ্বদিকে উন্নতির পথে চলে না। …কিন্তু ঐ তালগাছে কোন সতেজ ব্রততী যেমন তাহকে বেড়িয়া বেড়িয়া উপরের দিকে উঠে, সেইরুপই মানুষের মন ও মানবের সমাজ ক্রমোন্নতির পথে চলিয়া থাকে। একটা লম্বা সরল খুটীর গায়ে নীচ হইতে উপর পর্যন্ত একগাছা দড়ি জড়াইতে হইলে যেমন তাহাকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া নিতে হয়, মানুষের মনের ও মানবসমাজের ক্রমবিকাশের পশ্বও কতকটা তারই মতন। এই গতির ঝোঁকটা সর্বদাই উন্নতির দিকে থাকিলেও, প্রতি তরেই, উপরে উঠিবার জন্যই, একটু করিয়া নীচেও নামিয়া আসিতে হয়। ইংরাজিতে এরূপ তির্যকগতির একটা বিশিষ্ট নাম আছে, ইহাকে পাইরাল মোষ (spiral motion) বলে। সমাজবিকাশের ক্রমও এইরূপ স্পাইর্যাল, একান্ত সরল নহে। …আপনার গতি-বেগের অবিচ্ছিন্নতা রক্ষা করিয়া এক স্তর হইতে অন্য স্তরে যাইতে হইলেই ঐ উর্ধ্বমুখী তির্যকগতির পথ অনুসরণ করিতে হয়।
বিপিনবাবুর আবিষ্কৃত এই উন্নতিতত্ত্ব যে নূতন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; কিন্তু সত্য কি না তাই হচ্ছে বিচার্য।
বিপিনবাবু বলেন যে, রজ্জুতে সর্পজ্ঞান সত্যজ্ঞান নয়, ভ্রম। এ কথা সৰ্ববাদীসম্মত। কিন্তু রজ্জুতে মতাজ্ঞান যে সত্যজ্ঞান, এরূপ বিশ্বাস করবার কারণ কি। রজ্জু জড়পদার্থ, এবং সতেজ ব্রততী সজীব পদার্থ। দড়ি বেচারার আপনার ‘গতিবেগ’ বলে কোনোরূপ গুণ কি দোষ নেই। ও-বস্তুকে ইচ্ছে করলে নীচে থেকে জড়িয়ে উপরে তুলতে পার, উপর থেকে জড়িয়ে নীচে নামাতে পার, লম্বা করে ফেলতে পার, তাল-পাকিয়ে রাখতে পার। রজ্জু উন্নতি অবনতি তির্যকগতি কি সরলগতি-কোনোরূপ গতির ধার ধারে না। বিপিনবাবু এ ক্ষেত্রে রজ্জুর যে ব্যবহার করেছেন তা জ্ঞানের গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।
তার পর বিপিনবাবু এ সত্যই-বা কোন বিজ্ঞান থেকে উদ্ধার করলেন যে, মানুষের মন ও মানবসমাজ উদ্ভিদজাতীয়? সাইকলজি এবং সোশিয়লজি যে বটানির অন্তর্ভূত, এ কথা তো কোনো কেতাবে-কোরানে লেখে না। তর্কের খাতিরে এই অদ্ভুত উদ্ভিদতত্ত্ব মেনে নিলেও সকল সন্দেহের নিরাকরণ হয় না। মনে স্বতই এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, মানুষের মন ও মানবসমাজ উদ্ভিদ হলেও ঐ দুই পদার্থ যে লতাজাতীয়, এবং বক্ষজাতীয় নয়, তারই-বা প্রমাণ কোথায়। গাছের মতো সোজাভাবে সরলরেখায় মাথাঝাড়া দিয়ে ওঠা যে মানবধর্ম নয়, কোন যুক্তি কোন প্রমাণের বলে বিপিনবাবু এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন তা আমাদের জানানো উচিত ছিল; কেননা পালমহাশয়ের আন্তবাক, আমরা বৈজ্ঞানিক সত্য বলে গ্রাহ্য করতে বাধ্য নই। উকি যে যুক্তি নয়, এ জ্ঞান বিপিনবাবুর থাকা উচিত। উত্তরে হয়তো তিনি বলবেন যে, উগতিমাত্রেই তির্যকগতি-এই হচ্ছে জাগতিক নিয়ম। ঊর্ধ্বগতিমাত্ৰকেই যে কর আকার ধারণ করতে হবে, জড়জগতের এমন কোনো বিধিনির্দিষ্ট নিয়ম আছে কি না জানি নে। যদি থাকে তো মানুষের মতিগতি যে সেই একই নিয়মের অধীন এ কথা তিনিই বলতে পারেন, যিনি জীবে জড় এম করেন।
আপনার গতিবেগের অবিচ্ছিন্নতা রক্ষা করিয়া এক স্তর হইতে অন্য তর যাইতে হইলেই ঐ উদ্ধর্মখী তির্যকগতির পথ অনুসরণ করিতে হয়।
বিপিনবাবুর এই মত যে সম্পূর্ণ ভুল তা তাঁর প্রদর্শিত উদাহরণ থেকেই প্রমাণ করা যায়। ‘তালগাছ যে সরলরেখার ন্যায় ঊদ্ধদিকে উঠে’-তার থেকে এই প্রমাণ হয় যে, যে নিজের জোরে ওঠে সে সিধেভাবেই ওঠে; আর যে পরকে আশ্রয় করে ওঠে সেই পেঁচিয়ে ওঠে, যথা, তরুর আশ্রিত লতা।
দশ ছত্র রচনার ভিতর ডাইনামিকস বটানি সোশিয়লজি সাইকলজি প্রতি নানা শাস্ত্রের নানা সূত্রের এহেন জড়াপটকি বাধানো যে সম্ভব, এ জ্ঞান আমার ছিল না। সম্ভবত পালমহাশয় যে নূতন দৃষ্টি নিয়ে ঘরে ফিরেছেন, সেই দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে যে, স্বর্গের সিঁড়ি গোল সিঁড়ি। যদি তাই হয়, তা হলে এ কথাও মানতে হবে যে, পাতালের সিঁড়িও গোল; কারণ ওঠা-নামার জাগতিক নিয়ম অবশ্যই এক। সুতরাং ঘুরপাক খাওয়ার অর্থ ওঠাও হতে পারে, নামাও হতে পারে। এ অবস্থায় উন্নতিশীলের দল যদি কুটিল পথে না চলে সরল পথে চলতে চান, তা হলে তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না।
.
৫.
বিপিনবাবু যে তাঁর প্রবন্ধের বৈজ্ঞানিক পর্যায়ে নানারূপ পরস্পর-বিরোধী বাক্য একত্র করতে কুণ্ঠিত হন নি তার কারণ তিনি ইউরোপীয় দর্শন হতে এমন-এক সত্য উদ্ধার করেছেন, যার সাহায্যে সকল বিরোধের সমন্বয় হয়। হেগেলের থিসিস অ্যান্টিথিসিস এবং সিনথেসিস, এই বিপদের ভিতর যখন ত্রিলোক ধরা পড়ে, তখন তার অন্তর্ভূত সকল লোক যে ধরা পড়বে তার আর আশ্চর্য কি। হেগেলের মতে লজিকের নিয়ম এই যে, ‘ভাব’ (being) এবং ‘অভাব’ (non-being) এই দুটি পরস্পরবিরোধী-এবং এই দুয়ের সমন্বয়ে যা দাঁড়ায় তাই হচ্ছে ‘স্বভাব’ (beconting)। মানুষের মনের সকল ক্রিয়া এই নিয়মের অধীন, সুতরাং সৃষ্টিপ্রকরণও এই একই নিয়মের অধীন, কেননা এ জগৎ চৈতন্যের লীলা। অর্থাৎ তার লজিক এবং ভগবানের লজিক যে একই বস্তু, সে বিষয়ে হেগেলের মনে কোনোরূপ দ্বিধা ছিল না। তার কারণ হেগেলের বিশ্বাস ছিল যে, তিনি ভগবানের শুধু অবতার নন–স্বয়ং ভগবান। হেগেলের এই ঘরের খবর তাঁর সপ্রতিভ শিষ্য কবি হেনরি হাইনের (Henri Heine) গুরুমারাবিদ্যের গুণে ফাঁস হয়ে গেছে। বিপিনবাবুরও বোধ হয় বিশ্বাস যে, হেগেলের কথা হচ্ছে দর্শনের শেষকথা। সে যাই হোক, হেগেলের এই পশ্চিম-মীমাংসার বলে বিপিনবাবু, নুতন ও পুরাতনের সমন্বয় করতে চান। তিনি অবশ্য শুধু সূত্র পরিয়ে দিয়েছেন, তার প্রয়োগ করতে হবে আমাদের।
.
৬.
হেগেলের মত একে নতুন তার উপর বিদেশী; সুতরাং পাছে তা গ্রাহ্য করতে আমরা ইতস্তত করি এই আশঙ্কায় তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, হেগেলও যা, বেদান্তও তাই, সাংখ্যও তাই।
সমন্বয় অর্থে বিপিনবাবু কি বোঝেন, তার পরিচয় তিনি নিজেই দিয়েছেন। তাঁর মতে–
সমন্বয় মাত্রেই যে-বিরোধের নিষ্পত্তি করিতে যায়, তার বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষেরই দাবী-দাওয়া কিছু কাটিয়া হাটিয়া, একটা মধ্যপথ ধরিয়া তাঁহার ন্যায্য মীমাংসা করিয়া দেয়।
অর্থাৎ থিসিসকে কিছু ছাড়তে এবং অ্যান্টিথিসিসকে কিছু ছাড়তে হবে, তবে সিনথেসিস ডিক্রি পাবে। তাঁর দর্শনের এ ব্যাখ্যা শুনে সম্ভবত হেগেলের চক্ষুস্থির হয়ে যেত; কেননা তাঁর সিনথেসিস, কোনোরূপ রফাছাড়ের ফল নয়। তাতে থিসিস এবং অ্যান্টিথিসিস দুটিই পুরামাত্রায় বিদ্যমান; কেবল দুয়ে মিলিত হয়ে একটি নূতন মূর্তি ধারণ করে। সিনথেসিসের বিশ্লেষণ করেই থিসিস এবং অ্যান্টিথিসিস পাওয়া যায়। এর আধখানা এবং ওর আধখানা জোড়া দিয়ে অর্ধনারীশ্বর গড়া হেগেলের পদ্ধতি নয়।
তার পর মীমাংসা অর্থে যদি রফাছাড়ের নিষ্পত্তি হয় তা হলে বলতেই হবে যে, বিপিনবাবুর মীমাংসার সঙ্গে ব্যাস-জৈমিনির মীমাংসার কোনোই সম্পর্ক নেই। বেদান্তের মীমাংসা আর যাই হোক, আপস-মীমাংসা নয়। বেদান্তদর্শন নিজের দাবির এক-পয়সাও ছাড়ে নি, কোনো বিরোধী মতের দাবির এক-পয়সাও মানে নি। উত্তর-মীমাংসাতে অবশ্য সময়ের কথা আছে, কিন্তু সে সময়ের অর্থ যে কি, তা শংকর অতি পরিষ্কার ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন
এ সূত্ৰ বেদান্তবাক্যরূপ কুসুম গাঁথিবার সূত্র, অনুমান বা যুক্তি গাঁথিবার নহে ইহাতে নানাস্থানস্থ বেদান্তবাক্য-সকল আহৃত হইয়া মীমাংসিত হইবে।
এবং শংকরের মতে মীমাংসার অর্থ ‘অবিরোধী তর্কের সহিত বেদান্ত বাক্যসমূহের বিচার’। এ বিচারের উদ্দেশ্য এই প্রমাণ করা যে, বেদান্ত-বাক্যসমূহ পরস্পরবিরোধী নয়। হেগেলের পশ্চিম-মীমাংসার সহিত ব্যাসের উত্তর-মীমাংসার কোনো মিল নেই; না মতে, না পদ্ধতিতে। ব্রহ্মসূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় পরব্রহ্ম, হেগেলের প্রতিপাদ্য বিষয় অপরব্রহ্ম। নিরুক্তের মতে ভাববিকার ছয়প্রকার, যথা: সৃষ্টি স্থিতি হ্রাস বৃদ্ধি বিপর্যয় ও লয়। শংকর হ্রাস বৃদ্ধি ও বিপর্যয়কে গণনার মধ্যে আনেন নি, কেননা তাঁর মতে এ তিনটি হচ্ছে স্থিতিকালের ভাববিকার। অপর পক্ষে এই তিনটি ভাবই হচ্ছে হেগেলের অবলম্বন, কেননা তাঁর অ্যাবসলিউট হচ্ছে ইটর্নল্ বিকামিং। সুতরাং হেগেলের ব্রহ্ম শুধু অপরব্রহ্ম নন, তিনি ঐতিহাসিক ব্রহ্ম—অর্থাৎ ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ক্রমবিকাশ হচ্ছে। হেগেলের মতে তার সমসাময়িক ব্রহ্ম প্রুশিয়া-রাজ্যে বিগ্রহবান হয়েছিলেন। শংকর যে-জ্ঞানের উল্লেখ করেছেন, সে-জ্ঞান মানসিক ক্রিয়া নয়; অপর পক্ষে হেগেলের জ্ঞান ক্রিয়ারই যুগপৎ কর্তা ও কর্ম।
বেদান্তের মতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবার উপায় যুক্তি নয়; অপর পক্ষে হেগেলের মতে যুক্তির উপরেই ব্রহ্মের অস্তিত্ব নির্ভর করে। থিসিস এবং অ্যান্টিথিসিসের সুতোয় সততায় গেরো দিয়েই এক-একটি ব্রহ্মমহর্ত পাওয়া যায়। বেদান্তের ব্রহ্ম স্থির-বর্তমান, হেগেলের ব্রহ্ম চির-বর্ধমান-অর্থাৎ একটি স্ট্যাটিক অপরটি ডাইনামিক। আসল কথা এই যে, বেদান্ত যদি থিসিস হয়, তা হলে হেগেল তার অ্যান্টিথিসিস-এ দুই মতের অভেদ জ্ঞান শুধু অজ্ঞানের পক্ষে সম্ভব।
.
৭.
বিপিনবাবুর হাতে পড়ে শুধু বাদরায়ণ নয়, কপিলও হেগেলে লীন হয়ে গেছেন।
বিপিনবাবু আবিষ্কার করেছেন যে, যার নাম থিসিস অ্যান্টিথিসিস এবং সিনথেসিস, তারই নাম তমঃ রজঃ ও সত্ত্ব। কেননা তার মতে থিসিসের বাংলা হচ্ছে স্থিতি, অ্যান্টিথিসিসের বাংলা বিরোধ, এবং সিনথেসিসের বাংলা সমন্বয়। এ অনুবাদ অবশ্য গায়ের জোরে করা। কেননা, থিসিস যদি স্থিতি হয় তা হলে অ্যান্টিথিসিস অ-স্থিতি (গতি) এবং সিনথেসিস সংস্থিতি। সে যাই হোক, সাংখ্যের ত্রিগুণের সঙ্গে অবশ্য হেগেলের ত্রিসূত্রের কোনো মিল নেই; কেননা সাংখ্যের মতে এই ত্রিগুণের সমন্বয়ে জগতের লয় হয়, সৃষ্টি হয় না। সত্ত্ব রজঃ তমের মিলন নয়, বিচ্ছেদই হচ্ছে সৃষ্টির কারণ; অপর পক্ষে হেগেলের মতে থিসিস এবং অ্যান্টিথিসিসের মিলনের ফলে জগৎ সৃষ্ট হয়। বিপিনবাবুর ন্যায় পর্ব পশ্চিম সকল দর্শনের সমন্বয়কারের কাছে অবশ্য এ-সকল পার্থক্য তুচ্ছ এবং অকিঞ্চিৎকর; অতএব সর্বথা উপেক্ষণীয়।
তমঃ ও রজের মিলনে যে বহু জন্মলাভ করে, তা হেগেলের সিনথেসিস হতে পারে, কিন্তু তা সাংখ্যের সত্ত্ব নয়। এ কথা দুটি-একটি উদাহরণের সাহায্যে সহজেই প্রমাণ করা যেতে পারে। আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষের মন ও মানবসমাজের উন্নতির পদ্ধতি। বিপিনবাবুর উদভাবিত কপিল-হেগেল-দর্শন-অনুসারে ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়ায়–
তামসিক মন=সুপ্ত
রাজসিক মন =জাগ্রত
সাত্ত্বিক মন=ঝিমন্ত
তামসিক সমাজ=মৃত
রাজসিক সমাজ=জীবিত
সাত্ত্বিক সমাজ=জীবন্মৃত
অর্থাৎ সমন্বয়ের ফলে রজোগুণের উন্নতি নয়, অবনতি হয়। সগুণ যে তমোগ এবং রজোগণের মাঝামাঝি একটি পদার্থ এ কথা সাংখ্যাচার্যেরা অবগত নন, কেননা তারা হেগেল পড়েন নি। উক্ত দর্শনের মতে সত্ত্বগুণ রজোগুণের অতিরিক্ত, অন্তর্ভুত নয়। সাত্ত্বিক ভাব যে বিরোধের ভাব নয়, তার কারণ রজোগুণ যখন তমোগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হয় তখনই তা সত্ত্বগণে পরিণত হয়। হেগেলের মত অবশ্য সাংখ্যমতের সম্পূর্ণ বিপরীত। সাংখ্যকে উলটে ফেললে যা হয়, তারই নাম হেগেল-দর্শন। সাংখ্যমতে সক্ষম অনলোমরুমে স্বল হয়, হেগেল-মতে ঐ একই পদ্ধতিতে প্রল সক্ষম হয়। সাংখ্যের প্রকৃতি হেগেলের পুষ। সাংখ্যের মতে সৃষ্টিতে প্রকৃতি বিকারগ্রস্ত হন, হেগেলের মতে পুরুষ সাকার হন।
বিপিনবাবু দেশী-বিলাতি-দর্শনের সমন্বয় করে যে মীমাংসা করেছেন সে হচ্ছে অপুর্ব মীমাংসা; কেননা, কি স্বদেশে, কি বিদেশে, ইতিপূর্বে এরূপ অন্তর্ভূত মীমাংসা আর কেউ করেন নি।
নূতন-পুরাতনের সমন্বয়ের এই যদি নমুনা হয় তা হলে নূতন ও পুরাতন উভয়েই সমন্বয়কারকে বলবে—ছেড়ে দে বাবা, লড়ে বাঁচি।
বিপিনবাবু, যাকে সমন্বয় বলেন, বাংলা ভাষায় তার নাম খিচুড়ি।
সমাজদেবতার নিকটে পালমহাশয় যে খিচুড়িভোগ নিবেদন করে দিয়েছেন, যিনি তার প্রসাদ পাবেন তার যে কৃষ্ণতি হবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।
আসল কথা এই যে, দর্শনবিজ্ঞানের মোটা কথার আশ্রয় নেওয়ার অর্থ হচ্ছে কোনো বিশেষ সমস্যার মীমাংসা করা নয়, তার কাছ থেকে পলায়ন করা। দর্শন কি বিজ্ঞান যে আজ পর্যন্ত এমন-কোনো সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করেন নি যার সাহায্যে কোনো বিশেষ বিষয়ের বিশেষ মীমাংসা করা যায়, তার কারণ সকল বিশেষ বস্তুর বিশেষত্ব বাদ দিয়েই সর্বসাধারণে গিয়ে পৌছোনা যায়। বিশ্বকে নিঃস্ব করেই দার্শনিকেরা বিশ্বতত্ত্ব লাভ করেন। সোনা ফেলে আঁচলে গিট দেওয়াই দার্শনিকদের চিরকেলে অভ্যাস। এ উপায়ে সম্ভবত ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভ হতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান লাভ হয় না। সমাজের উন্নতি দেশকালপাত্র-সাপেক্ষ, সুতরাং দেশকালের অতীত কিংবা সর্বদেশে সর্বকালে সমান বলবৎ কোনো সত্যের দ্বারা সে উন্নতি সাধন করবার চেষ্টা বৃথা। ফিজিক্স কিংবা মেটাফিজিক্সএর তত্ত্ব সমাজতত্ত্ব নয়, এবং এ দুই তত্ত্ব যে পৃথক জাতীয় তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিপিনবাবুর আবিষ্কৃত ঊর্ধ্বগতির দৃষ্টান্ত থেকেই দেখানো যেতে পারে। এমন-কোনো জাগতিক নিয়ম নেই যে, মানুষের চেষ্টা ব্যতিরেকেও তার উন্নতি হবে। হ্রাস বৃদ্ধি ও বিপর্যয়, এ তিনই জীবনের ধর্ম; সুতরাং সমাজের উন্নতি ও অবনতি মানুষের দ্বারাই সাধিত হয়। মানবের ইচ্ছাশক্তিই মানবের উন্নতির মূল কারণ। তা ছাড়া মানবের উন্নতি যে ক্রমোন্নতি হতে বাধ্য, এমন-কোনো নিয়মের পরিচয় ইতিহাস দেয় না। বরং ইতিহাস এই সত্যের পরিচয় দেয় যে, বিপর্যয়ের ফলেই মানব অনেক সময়ে মহা উন্নতি লাভ করেছে। যে-সব মহাপুরুষকে আমরা ঈশ্বরের অবতার বলে মনে করি, যথা বুদ্ধদেব যিশুখৃস্ট মহম্মদ চৈতন্য প্রভুতি এরা মানুষের মনকে বিপর্যস্ত করেই মানবসমাজকে উন্নত করেছেন; এরা পাইরাল, মোশনএর ধার ধারতেন না কিংবা স্থিতি ও গতির মধ্যে দূতীগিরি করে তাদের মিলন ঘটানো নিজেদের কর্তব্য বলে মনে করেন নি।
মানুষের মনকে যদি গেরোবাজের মতো আকাশে ডিগবাজি খেতে খেতে উঠতে হত, এবং মানবসমাজকে যদি লোটনের মতো মাটিতে লুটতে লুটতে এগোতে হত, তা হলে এ দুয়ের বেশিক্ষণ সে কাজ করতে হত না, দু দণ্ডেই তাদের ঘাড় লটকে পড়ত। সুতরাং কি মন কি সমাজ, কোনোটিকেই পাকচক্রের ভিতর ফেলবার আবশ্যকতা নেই। বিপিনবাবুর বক্তব্য যদি এই হয় যে, পৃথিবীতে অবাধগতি বলে কোনো জিনিস নেই, তা হলে আমরা বলি—এ সত্য শিশুতেও জানে যে পদে পদে বাধা অতিক্রম করেই অগ্রসর হতে হয়। তাই বলে স্থিতি-গতির সমন্বয় করে চলার অর্থ যে শুধু হামাগুড়ি দেওয়া, এ কথা শিশুতেও মানে না। অধোগতি অপেক্ষা উন্নতির পথে যে অধিকতর বাধা অতিক্রম করতে হয়, এ তো সর্বলোকবিদিত। কিন্তু এর থেকে এ প্রমাণ হয় না যে, স্থিতির বিরুদ্ধে গতি নামক ‘বিরোধটি জাগিয়ে’ রাখা মূর্খতা এবং সেটিকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়াটাই জ্ঞানীর কর্তব্য। জড়ের সঙ্গে যোঝাযুঝি করেই জীবন স্ফূর্তি লাভ করে। সুতরাং পুরাতন যে-পরিমাণে জড়, সেই পরিমাণে নবজীবনকে তার সঙ্গে লড়তে হবে। যে সমাজের যত অধিক জীবনীশক্তি আছে, সে সমাজে স্থিতিতে ও গতিতে জড়ে ও জীবে তত বেশি বিরোধের পরিচয় পাওয়া যাবে। নূতন-পুরাতনের এই বিরোধের ফলে যা ভেঙে পড়ে তার চাইতে যা গড়ে ওঠে, সমাজের পক্ষে তার মূল্য ঢের বেশি। কোনো নূতনের বরের ঘরের পিসি ও পুরাতনের কনের ঘরের মাসির মধ্যস্থতায় এ দুই পক্ষের ভিতর যে চিরশান্তি স্থাপিত হবে, এ আশা দুরাশা মাত্র।
আমি পূর্বে বলেছি যে, নূতন-পুরাতনে যদি কোথায়ও বিবাদ থাকে তো সে সাহিত্যে, সমাজে নয়। আমার বিশ্বাস যদি অন্যরূপ হত, তা হলে আমি বিপিনবাবুর কথার প্রতিবাদ করতুম না। তার কারণ, প্রথমত আমি সমাজসংস্কারব্যাপারে অব্যবসায়ী। অতএব এ ব্যাপারে কোন ক্ষেত্রে আক্রমণ করতে হয় এবং কোন ক্ষেত্রে পৃঠভঙ্গ দিতে হয় এবং কোনটি বিগ্রহের এবং কোনটি সন্ধির যুগ তা আমার জানা নেই। দ্বিতীয়ত, বিপিনবাবুর উদ্ভাবিত পদ্ধতি অনুসারে নূতন-পুরাতনের জমাখরচ করলে সামাজিক হিসাবে পাওয়া যায় শুধু শূন্য। সুতরাং কি নূতন, কি পুরাতন, কোনো পক্ষই ও-উপায়ে কোনো সামাজিক সমস্যার মীমাংসা করবার চেষ্টামাত্রও করবেন না। তৃতীয়ত, ডাক্তার শীলের মতে–
সহস্র বৎসরাবধি এই দেশ ঠিক সেই জায়গায়ই বসিয়া আছে; তার আর কোনও বিকাশ হয় নাই।
যে সমাজ হাজার বৎসর এক স্থানে এক ভাবে বসে আছে তার আসন টলাবার শক্তি আমাদের মতো সাহিত্যিকের শরীরে নেই। বিপিনবাবুর মতামত কর্মকাণ্ডের নয়, জ্ঞানকাণ্ডের বস্তু বলেই এ বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছি। তাঁর বর্ণিত সময়ের কোনো সার্থকতা সমাজে থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু সাহিত্যে নেই। সামাজিক ক্রিয়াকর্মে দুধের সঙ্গে জলের সমন্বয়-প্ৰচলন দেখা যায়। কিন্তু তাই বলে সাহিত্যে জলোদুধের আমদানি আমরা বিনা আপত্তিতে গ্রাহ্য করতে পারি নে। কারণ ও-বস্তু অন্তরাত্মার পখকে মুখরোচকও নয়, স্বাস্থ্যকরও নয়। অথচ সরস্বতীর মন্দিরে কিঞ্চিৎ আর কিঞ্চিৎ মদের সমন্বয় যে জ্ঞানামৃত বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে, তার প্রমাণ তো হাতে-হাতেই পাওয়া যাচ্ছে। সাহিত্যের এই পাঞ্চ্ পান করে আমাদের সমাজের আজ মাথা ঘুরছে। এই ঘুরুনির চোটে অনেকে চোখে এত ঝাপসা দেখেন যে, কোন বস্তু নূতন আর কোন বস্তু পুরাতন, কোনটি স্বদেশী আর কোনটি বিদেশী-তাও তারা চিনতে পারেন না। এ অবস্থায় বাঙালির প্রথম দরকার সমাজে নূতন-পুরাতনের সময় নয়, মনে নূতন-পুরাতনের বিচ্ছেদ ঘটানো। আমাদের শিক্ষা যাকে এক সঙ্গে গুলে ঘুলিয়ে দিচ্ছে, আমাদের সাহিত্যের কাজ হওয়া উচিত তাই বিশ্লেষণ করে পরিষ্কার করা।
পৌষ ১৩২১
————-
১. “নূতনে পুরাতনে”, ‘নারায়ণ’, অগ্রহায়ণ ১৩২১।
২. “হিন্দুর প্রকৃত হিন্দুত্ব”, অগ্রহায়ণ ১৩২১।