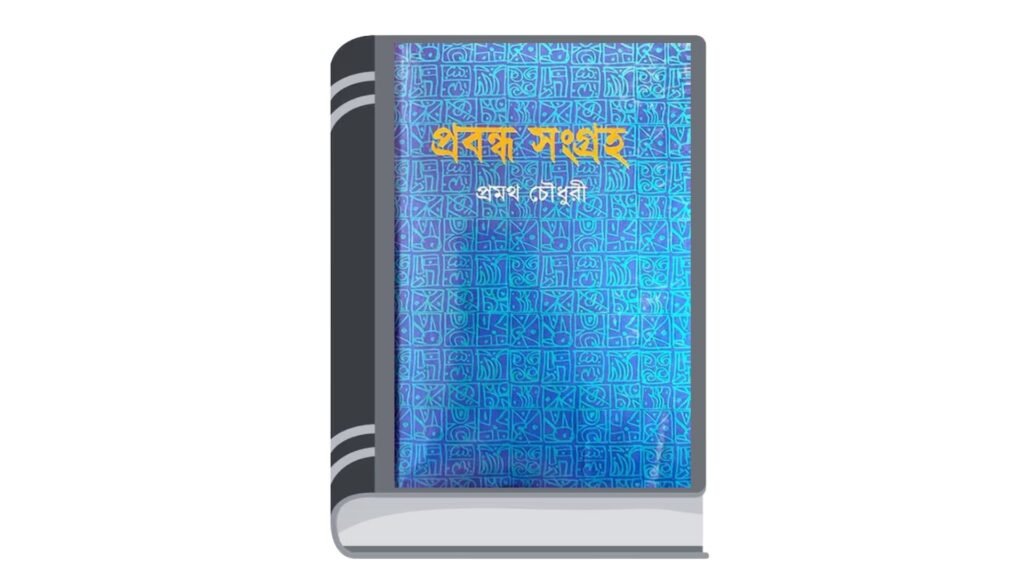রূপের কথা
রূপের কথা
এদেশে সচরাচর লোকে যা লেখে ও ছাপায় তাই যদি তাদের মনের কথা হয়, তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে, আমরা মানবসভ্যতার চরম পদ লাভ করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই প্রকাণ্ড সত্যটা বিদেশীরা মোটেই দেখতে পায় না। এটা সত্যিই দুঃখের বিষয়। কেননা, সভ্যতারও একটা চেহারা আছে; এবং যে সমাজের সচেহারা নেই, তাকে সুসভ্য বলে মানা কঠিন। বিদেশী বলতে দু শ্রেণীর লোক বোঝায়— এক পরদেশী, আর-এক বিলেতি। আমরা যে বড়-একটা কারও চোখে পড়ি নে, সেবিষয়ে এই দুই দলের বিদেশীই একমত।
যাঁরা কালাপানি পার হয়ে আসেন, তাঁরা বলেন যে, আমাদের দেশ দেখে তাঁদের চোখ জড়োয়, কিন্তু আমাদের বেশ দেখে সে চোখ ক্ষম হয়। এর কারণ, আমাদের দেশের মোড়কে রং আছে, আমাদের দেহের মোড়কে নেই। প্রকৃতি বাংলাদেশকে যে কাপড় পরিয়েছেন, তার রং সবুজ; আর বাঙালি নিজে যে কাপড় পরেছে, তার রং, আর যেখানেই পাওয়া যাক, ইন্দ্রধনুর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমরা আপাদমস্তক রং-ছট বলেই অপর কারও নয়নাভিরাম নই। সুতরাং যারা আমাদের দেশ দেখতে আসে, তারা আমাদের দেখে খুশি হয় না। যাঁর বোম্বাই-শহরের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় আছে, তিনিই জানেন কলকাতার সঙ্গে সে শহরের প্রভেদটা কোথায় এবং কত জাজল্যমান। সেদেশে জনসাধারণ পথেঘাটে সকালসন্ধ্যে রঙের ঢেউ খেলিয়ে যায় এবং সে রঙের বৈচিত্র্যের ও সৌন্দর্যের আর অন্ত নেই। কিন্তু আমাদের গায়ে জড়িয়ে আছে চির-গোধুলি; তাই শুধু বিলেতি নয়, পরদেশী ভারতবাসীর চোখেও আমরা এতটা দৃষ্টিকট। বাকি ভারতবর্ষ সাজসজ্জায় স্বদেশী, আমরা আধ-স্বদেশী হাফ-বিলেতি। আর বিলেতি মতে, হয় কালো নয় শাদা–নইলে সভ্যতার লজ্জা নিবারণ হয় না। রং চাই শুধু সং সাজবার জন্যে। আমাদের নবসভ্যতাও কার্যত এই মতে সায় দিয়েছে।
২.
আপনারা বলতে পারেন যে, একথা যদি সত্যও হয়, তাতে আমাদের কি যায়-আসে। বিদেশীর মনোরঞ্জন করবার জন্য আমরা তো আর জাতকে-জাত আমাদের পরন-পরিচ্ছদ আমাদের হাল-চাল সব বদলে ফেলতে পারি নে? জীবনযাত্রা ব্যাপারটা তো আর অভিনয় নয় যে, দর্শকের মুখ চেয়ে সে-জীবন গড়তে হবে এবং তার উপর আবার রং ফলাতে হবে। একথা খুব ঠিক। জীবন আমরা কিসের জন্য ধারণ করি তা না জানলেও, এটা জানি যে, পরের জন্য আমরা তা ধারণ করি নে–অপর দেশের অপর লোকের জন্য তো নয়ই। তবে বিদেশীর কথা উত্থাপন করবার সার্থকতা এই যে, জাতীয়জীবনের একটি বিদেশীর চোখে যেমন একনজরে ধরা পড়ে, স্বদেশীর চোখে তা পড়ে না। কেননা, আজন্ম দেখে দেখে লোকের চোখে যা সয়ে গেছে, যারা প্রথম দেখে তাদের চোখে তা সয় না।
এই বিদেশীরাই আমাদের সজ্ঞান করে দিয়েছে যে, রূপ সম্বন্ধে আমরা চোখ থাকতেও কানা। আমাদের রূপজ্ঞান যে নেই, কিংবা যদি থাকে তো অতি কম, সেবিষয়ে বোধ হয় কোনো মতভেদ নেই। কেননা, এ জ্ঞানের অভাবটা আমরা জাতীয় মনের দৈন্য বলে মনে করি নে। বরং সত্যকথা বলতে গেলে, আমাদের বিশ্বাস যে, এই রূপান্ধতাটাই আমাদের জাতীয় চরিত্রের মহত্ত্বের পরিচয় দেয়। রূপ তো একটা বাইরের জিনিস; শুধু তাই নয়, বাহ্যবস্তুরও বাইরের জিনিস; ও জিনিসকে যারা উপেক্ষা, এমনকি অবজ্ঞা, করতে না শিখেছে তারা আধ্যাত্মিকতার সন্ধান জানে না। আর আমরা আরকিছু হই আর না-হই, বালবৃদ্ধবনিতা সকলেই যে আধ্যাত্মিক। সেকথা যে অস্বীকার করবে, সে নিশ্চয়ই স্বদেশ এবং স্বজাতিদ্রোহী।
৩.
রপ-জিনিসটাকে যাঁরা একটা পাপ মনে করেন, তাঁদের মতে অবশ্য রুপের প্রশ্রয় দেওয়ার অর্থ পাপের প্রশ্রয় দেওয়া। কিন্তু দলে পাতলা হলেও পৃথিবীতে এমনসব লোক আছে, যারা রূপকে মান্য করে শ্রদ্ধা করে, এমনকি পুজো করতেও প্রস্তুত; অথচ নিজেদের মহাপাপী মনে করে না। এই রূপেভক্তের দল অবশ্য স্বদেশীর কাছে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য, অর্থাৎ প্রমাণপ্রয়োগ-সহকারে রুপের স্বত্বসাব্যস্ত করতে বাধ্য। আপসোসের কথা এই যে, যে সত্য সকলের প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত, সেই সত্য এদেশে প্রমাণ করতে হয়— অর্থাৎ একটা সহজ কথা বলতে গেলে, আমাদের ন্যায়-অন্যায়ের স্রোতের উজান ঠেলে যেতে হয়।
যা সকলে জানে–আছে, তা নেই বলাতে অতিবন্ধির পরিচয় দেওয়া হতে পারে, কিন্তু বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা এই ‘অতি’র অতিভক্ত হওয়াতে আমাদের ইতির জ্ঞান নষ্ট হয়েছে।
বস্তুর রূপে বলে যে একটি ধর্ম আছে, এ হচ্ছে শোনা-কথা নয়। দেখাজিনিস। যাঁর চোখ-নামক ইন্দ্রিয় আছে, তিনিই কখনো-না-কখনো তার সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। এবং আমাদের সকলেরই চোখ আছে; সম্ভবত শুধু তাঁদের ছাড়া, যাঁরা সৌন্দর্যের নাম করলেই অতীন্দ্রিয়তার ব্যাখ্যান অর্থাৎ উপাখ্যান শর, করেন। কিন্তু আমি এই রূপ-জিনিসটিকে অতিবজিত ইন্দ্রিয়ের কোঠাতেই টিকিয়ে রাখতে চাই; কেননা, অতীন্দ্রিয়-জগতে রূপ নিশ্চয়ই অরূপ হয়ে যায়।
৪.
রূপের বিষয় দার্শনিকেরা কি বলেন আর না-বলেন, তাতে কিছু যায়আসে না; কেননা, যা দৃষ্টির অগোচর, তাই দর্শনের বিষয়। অতএব একথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, বস্তুর রূপ বলে যে একটি গুণ আছে, তা মানুষমাত্রেই জানে এবং মানে। তবে সেই গুণের পক্ষপাতী হওয়াটা গুণের কি দোষের— এই নিয়েই যা মতভেদ।
রূপকে আমরা ভক্তি করি নে, সম্ভবত ভালোবাসি নে। আপনারা সকলেই জানেন যে, হালে একটা মতের বহুলপ্রচার হয়েছে, যার ভিতরকার কথা এই যে, জাতীয় আত্মমর্যাদা হচ্ছে পরশ্রীকাতরতারই সদর পিঠ। সম্ভবত একথা সত্য, কিন্তু তাই বলে শ্রীকাতরতাও যে ঐ জাতীয় আত্মমর্যাদার লক্ষণ একথা স্বীকার করা যায় না; কেননা, বিশ্বমানবের সভ্যতার ইতিহাস এর বিরদ্ধে চিরদিন সাক্ষি দিয়ে আসছে।
স্বদেশের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেলেই অপর সভ্যজাতির কাছে রূপের মর্যাদা যে কত বেশি, তার প্রমাণ হাতে-হাতে পাওয়া যাবে। বর্তমান ইউরোপ সুন্দরকে সত্যের চাইতে নীচে আসন দেয় না, সেদেশে জ্ঞানীর চাইতে আর্টিস্টের মান্য কম নয়। তারা সভ্যসমাজের দেহটাকে অর্থাৎ দেশের রাস্তাঘাট বাড়িঘরদোর মন্দিরপ্রাসাদ, মানুষের আসনবসন সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি নিত্য নূতন করে সুন্দর করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করছে। সে চেষ্টার ফল স, কি কু হচ্ছে, সে স্বতন্ত্র কথা। ইউরোপীয় সভ্যতার ভিতর অবশ্য একটা কুৎসিত দিক আছে, যার নাম কমার্শিয়ালিজম; কিন্তু এই দিকটে কদর্য বলেই তার সর্বনাশের দিক। কমার্শিয়ালিজম,এর মূলে আছে লোভ। আর লোভে পাপ পাপে মৃত্যু। আপনারা সকলেই জানেন যে, রূপের সঙ্গে মোহের সম্পর্ক থাকতে পারে, কিন্তু লোভের নেই।
ইউরোপ ছেড়ে এশিয়াতে এলে দেখতে পাই যে, চীন ও জাপান রূপের এতই ভক্ত যে, রুপের আরাধনাই সেদেশের প্রকৃত ধর্ম বললেও অত্যুক্তি হয় না। রূপের প্রতি এই পরাপ্ৰীতিবশত চীনজাপানের লোকের হাতে-গড়া এমন জিনিস নেই যার রূপ নেই–তা সে ঘটিই হোক আর বাটিই হোক। যাঁরা তাদের হাতের কাজ দেখেছেন, তাঁরাই তাদের রূপ-সৃষ্টির কৌশল দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন। মোঙ্গলজাতিকে ভগবান রূপ দেন নি, সম্ভবত সেই কারণে সন্দরকে তাদের নিজের হাতে গড়ে নিতে হয়েছে। এই তো গেল বিদেশের কথা।
৫.
আবার শুধু স্বদেশের নয়, সকালের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেলে আমরা ঐ একই সত্যের পরিচয় পাই। প্রাচীন গ্রীকো-ইতালীয় সভ্যতার ঐকান্তিক রূপচর্চার ইতিহাস তো জগৎবিখ্যাত। প্রাচীন ভারতবর্ষও রূপ সম্বন্ধে অন্ধ ছিল না; কেননা, আমরা যাই বলি নে কেন, সে সভ্যতাও মানবসভ্যতা–একটা সৃষ্টিছাড়া পদার্থ নয়। সে সভ্যতারও শুধু আত্মা নয়, দেহ ছিল; এবং সে দেহকে আমাদের পপুরুষেরা সুঠাম ও সুন্দর করেই গড়তে চেষ্টা করেছিলেন। সে দেহ আমাদের চোখের সম্মুখে নেই বলেই আমরা মনে করি যে, সেকালে যা ছিল তা হচ্ছে শুধু অশরীরী আত্মা। কিন্তু সংস্কৃতসাহিত্য থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাঁদের কতটা সৌন্দর্য জ্ঞান ছিল। আমরা যাকে সংস্কৃতকাব্য বলি, তাতে রূপবর্ণনা ছাড়া আর বড়-কিছু নেই; আর সে রূপবর্ণনাও আসলে দেহের, বিশেষত রমণী-দেহের, বর্ণনা; কেননা, সে কাব্যসাহিত্যে যে প্রকৃতিবর্ণনা আছে তাও বস্তুত রমণীর রূপবর্ণনা। প্রকৃতিকে তাঁরা সুন্দরী রমণী হিসেবেই দেখেছিলেন। তার যে অংশ নারীঅঙ্গের উপমেয় কি উপমান নয়, তার স্বরূপ হয় তাঁদের চোখে পড়ে নি, নয় তা তাঁরা রূপ বলে গ্রাহ্য করেন নি। সংস্কৃতসাহিত্যে হরেকরকমের ছবি আছে, কিন্তু ল্যাণ্ডসকেপ নেই বললেই হয়; অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক প্রকৃতির অস্তিত্বের বিষয় তাঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। ল্যাণ্ডসকেপ প্রাচীন গ্রীস কিংবা রোমের হাত থেকেও বেরয় নি। তার কারণ, সেকালে মানুষে মানুষে বাদ দিয়ে বিশ্বসংসার দেখতে শেখে নি। এর প্রমাণ শুধু আটে নয়, দর্শনে-বিজ্ঞানেও পাওয়া যায়। আমরা আমাদের নববিজ্ঞানের প্রসাদে মানুষকে এ বিশ্বের পরমাণুতে পরিণত করেছি, সম্ভবত সেই কারণে আমরা মানবদেহের সৌন্দর্য অবজ্ঞা করতে শিখেছি। আমাদের পূর্বপুরুষেরা কিন্তু সে সৌন্দর্যকে একটি অমূল্য বস্তু বলে মনে করতেন; শুধু স্ত্রীলোকের নয়, পুরুষের রূপের উপরও তাঁদের ভক্তি ছিল। যাঁর অলোকমান্য রূপ নেই, তাঁকে এদেশে পুরাকালে মহাপুরুষ বলে কেউ মেনে নেয় নি। শ্রীরামচন্দ্র বুদ্ধদেব শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারেরা সকলেই সৌন্দর্যের অবতার ছিলেন। রূপগণের সন্ধিবিচ্ছেদ করা সেকালের শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ ছিল না। শুধু তাই নয়, আমাদের পূর্বপুরুষদের কদাকারের উপর এতটাই ঘণা ছিল যে, পরাকালের শদ্রেরা যে দাসত্ব হতে মুক্তি পায় নি, তার একটি প্রধান কারণ তারা ছিল কৃষ্ণবর্ণ এবং কুৎসিত অন্তত আর্যদের চোখে। সেকালের দর্শনের ভিতর অরূপের জ্ঞানের কথা থাকলেও সেকালের ধর্ম রূপজ্ঞানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। পরব্রহ নিরাকার হলেও ভগবান, মন্দিরে মন্দিরে মতিমান। প্রাচীন মতে নির্গুণ-ব্রহ্ম অরূপ এবং সগুণ-ব্রহ্ম স্বরূপ।
৬.
সভ্যতার সঙ্গে সৌন্দর্যের এই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকবার কারণ, সভ্যসমাজ বলতে বোঝায় গঠিত-সমাজ। যে সমাজের গড়ন নেই, তাকে আমরা সভ্যসমাজ বলি নে। একালের ভাষায় বলতে হলে সমাজ হচ্ছে একটি অর্গানিজম; আর আপনারা সকলেই জানেন যে সকল অর্গানিজম, একজাতীয় নয়, ও-বস্তুর ভিতর উচুনিচুর প্রভেদ বিস্তর। অর্গানিক-জগতে প্রোটোপ্ল্যাজম হচ্ছে সবচাইতে নীচে এবং মানুষ সবচাইতে উপরে। এবং মানুষের সঙ্গে প্রোটোপ্ল্যাজম এর প্রত্যক্ষ পার্থক্য হচ্ছে রূপে; অপর-কোনো প্রভেদ আছে কি না, সে হচ্ছে তর্কের বিষয়। মানুষে যে প্রোটোপ্ল্যাজম,এর চাইতে রূপবান, এবিষয়ে, আশা করি, কোনো মতভেদ নেই। এই থেকে প্রমাণ হয় যে, যে সমাজের চেহারা যত সুন্দর, সে সমাজ তত সভ্য। এরূপ হবার একটি স্পষ্ট কারণও আছে। এ জগতে রূপ হচ্ছে শক্তির চরম বিকাশ; সমাজ গড়বার জন্য মানুষের শক্তি চাই এবং সুন্দর করে গড়বার জন্য তার চাইতেও বেশি শক্তি চাই। সুতরাং মানুষ যেমন বাড়বার মুখে ক্ৰমে অধিক সশ্রী হয়ে ওঠে এবং মরবার মুখে ক্রমে অধিক কুশ্রী হয় জাতের পক্ষেও সেই একই নিয়ম খাটে। কদর্যতা দুর্বলতার বাহ্য লক্ষণ, সৌন্দর্য শক্তির। এই ভারতবর্ষের অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই দেখা যায় যে, যখনই দেশে নবশক্তির আবির্ভাব হয়েছে তখনই মঠে-মন্দিরে-বেশে-ভূষায় মানুষের আশায়-ভাষায় নবসৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। ভারতবর্ষের আর্টের বৌদ্ধযুগ ও বৈষ্ণবযুগ এই সত্যেরই জাজল্যমান প্রমাণ।
আমাদের এই কোণঠাসা দেশে যেদিন চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয়, সেইদিনই বাঙালি সৌন্দর্যের আবিষ্কার করে। এর পরিচয় বৈষ্ণবসাহিত্যে পাওয়া যায়। কিন্তু সে সৌন্দর্যবৃদ্ধি যে টিকল না, বাংলার ঘরেবাইরে যে তা নানারূপে নানা আকারে ফটল না তার কারণ চৈতন্যদেব যা দান করতে এসেছিলেন তা ষোলোআনা গ্রহণ করবার শক্তি আমাদের ছিল না। যে কারণে বাংলার বৈষ্ণবধর্ম বাঙালিসমাজকে একাকার করবার চেষ্টায় বিফল হয়েছে, হয়ত সেই একই কারণে তা বাঙালিসভ্যতাকে সাকার করে তুলতে পারে নি। ভক্তির রস আমাদের বুকে ও মুখে গড়িয়েছে, আমাদের মনে ও হাতে তা জমে নি। ফলে, এক গান ছাড়া আর-কিছুকেই আমরা নবরপ দিতে পারি নি।
৭.
এসব কথা যদি সত্য হয়, তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে, আমাদের রূপজ্ঞানের অভাবটা আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেয় না। কিন্তু একথা মুখ ফটে বললেই আমাদের দেশের অন্ধের দল লগড় ধারণ করবেন। এর কারণ কি, তা বলছি।
সত্য ও সৌন্দর্য, এ দুটি জিনিসকে কেউ উপেক্ষা করতে পারেন না। হয় এদের ভক্তি করতে হবে, নয় অভক্তি করতে হবে। অর্থাৎ সত্যকে উপেক্ষা করলে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে; আর সুন্দরকে অবজ্ঞা করলে কুৎসিতের প্রশ্রয় দিতেই হবে। এ পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, তা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত এক স, আর-এক কু। সু-কে অর্জন না করলে কু-কে বর্জন করা কঠিন। আমাদের দশাও হয়েছে তাই। আমাদের সুন্দরের প্রতি যে অনুরাগ নেই, শুধু তাই নয়, ঘোরতর বিরাগ আছে।
আমরা দিনে-দুপুরে চীৎকার করে বলি যে, সাহিত্যে যে ফলের কথা জ্যোৎস্নার কথা লেখে সে লেখক নিতান্তই অপদার্থ।
এঁদের কথা শুনলে মনে হয় যে, সব ফলই যদি ডুমুর হয়ে ওঠে আর অমাবস্যা যদি বারোমেসে হয়, তাহলেই এ পৃথিবী ভূস্বর্গ হয়ে উঠবে; এবং সে স্বর্গে অবশ্য কোনো কবির স্থান হবে না। চন্দ্র যে সৌরমণ্ডলের মধ্যে একটি প্রক্ষিপ্ত গোলক, সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ও রিফ্লেক্টর ভগবান আকাশে ঝুলিয়ে দিয়েছেন; সুতরাং জ্যোৎস্না যে আছে, তার জন্য কবি দায়ী নন, দায়ী স্বয়ং ভগবান। কিন্তু এই জ্যোৎস্নাবিদ্বেষ থেকেই এদের প্রকৃত মনোভাব বোঝা যায়। এ রাগটা আসলে আলোর উপর রাগ। জ্ঞানের আলোক যখন আমাদের চোখে পরোপরি সয় না, তখন রূপের আলোক যে মোটেই সইবে না— তাতে আর বিচিত্র কি। জ্ঞানের আলো বস্তুজগৎকে প্রকাশ করে, সুতরাং এমন অনেক বস্তু প্রকাশ করে, যা আমাদের পেটের ও প্রাণের খোরাক যোগাতে পারে; কিন্তু রুপের আলো শুধু নিজেকেই প্রকাশ করে, সুতরাং তা হচ্ছে শুধু আমাদের চোখের ও মনের খোরাক। বলা বাহুল্য, উদর ও প্রাণ প্রোটোল্যাজম এরও আছে, কিন্তু চোখ ও মন শুধু মানুষেরই আছে। সুতরাং যাঁরা জীবনের অর্থ বোঝেন একমাত্র বেচে থাকা এবং তজ্জন্য উদরপতি করা, তাঁদের কাছে জ্ঞানের আলো গ্রাহ্য হলেও রূপের আলো অবজ্ঞাত। এ দুয়ের ভিতর প্রভেদও বিস্তর। জ্ঞানের আলো শাদা ও একঘেয়ে, অর্থাৎ ও হচ্ছে আলোর মূল; অপরপক্ষে, রূপের আলো রঙিন ও বিচিত্র, অর্থাৎ আলোর ফল। আদিম মানবের কাছে ফলের কোনো আদর নেই, কেননা ও-বস্তু আমাদের কোনো আদিম ক্ষুধার নিবৃত্তি করে না; ফলে আর-যাই হোক, চর্ব্য-চোষ্য কিংবা লেহ্য-পেয় নয়।
৮.
এসব কথা শুনে আমার বৈজ্ঞানিক বন্ধুরা নিশ্চয়ই বলবেন যে, আমি যা বলছি সেসব জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা নয়, সেরেফ কবিত্ব। বিজ্ঞানের কথা এই যে, যে আলোকে আমি শাদা বলছি, সেই হচ্ছে এ বিশ্বের একমাত্র অখণ্ড আলো; সেই সমস্ত আলো রিফ্র্যাকটেড অর্থাৎ ব্যস্ত হয়েই আমাদের চোখে বহুরুপী হয়ে দাঁড়ায়। তথাস্তু। এই রিফ্র্যাকশনএর একাধারে নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ হচ্ছে–পঞ্চভূতের বহির্ভূত ইথার-নামক রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শশব্দের অতিরিক্ত একটি পদার্থ। এবং এই হিল্লোলিত পদার্থের ধর্ম হচ্ছে এই জড়জগৎটাকে উৎফুল্ল করা, রুপান্বিত করা। রূপ যে আমাদের খুল-শরীরের কাজে লাগে না, তার কারণ বিশ্বের স্থূল-শরীর থেকে তার উৎপত্তি হয় নি। আমাদের ভিতর যে সক্ষম-শরীর অর্থাৎ ইথার আছে, বাইরের রূপের স্পর্শে সেই সুক্ষ-শরীর স্পন্দিত হয়, আনন্দিত হয়, পুলকিত হয়, প্রস্ফুটিত হয়। রূপজ্ঞানেই মানুষের জীবন্মক্তি, অর্থাৎ স্থূল-শরীরের বন্ধন হতে মুক্তি। রূপজ্ঞান হারালে মানুষ আজীবন পঞ্চভূতেরই দাসত্ব করবে। রূপবিদ্বেষটা হচ্ছে আত্মার প্রতি দেহের বিদ্বেষ, আলোর বিরুদ্ধে অন্ধকারের বিদ্রোহ। রূপের গুণে অবিশ্বাস করাটা নাস্তিকতার প্রথম সত্র।
৯.
ইন্দ্ৰিয়জ বলে বাইরের রূপের দিকে পিঠ ফেরালে ভিতরের রূপের সাক্ষাৎ পাওয়া কঠিন; কেননা, ইন্দ্রিয়ই হচ্ছে জড় ও চৈতন্যের একমাত্র বন্ধনসত্র। এবং ঐ সত্রেই রূপের জন্ম। অন্তরের রূপও যে আমাদের সকলের মনশ্চক্ষে ধরা পড়ে না, তার প্রমাণস্বরূপ একটা চলতি উদাহরণ নেওয়া যাক।
রবীন্দ্রনাথের লেখার প্রতি অনেকের বিরক্তির কারণ এই যে, সে লেখার রূপ আছে। রবীন্দ্রনাথের অন্তরে ইথার আছে, তাই সে মনের ভিতর দিয়ে যে ভাবের আলো রিফ্র্যাকটেড হয়ে আসে, তা ইন্দ্রধনুর বর্ণে রঞ্জিত ও ছন্দে মত হয়ে আসতে বাধ্য। স্থূলদর্শীর স্থূলষ্টিতে তা হয় অসত্য নয় অশিব বলে ঠেকা কিছু আশ্চর্য নয়।
মানুষে তিনটি কথাকে বড় বলে স্বীকার করে, তার অর্থ তারা বুঝুক আর না- বুঝুক। সে তিনটি হচ্ছে : সত্য শিব আর সুন্দর। যার রুপের প্রতি বিদ্বেষ আছে, সে সন্দরকে তাড়না করতে হলে হয় সত্যের নয় শিবের দোহাই দেয়; যদিচ সম্ভবত সে ব্যক্তি সত্য কিংবা শিবের কখনো একমনে সেবা করে নি। যদি কেউ বলেন যে, সুন্দরের সাধনা কর— অমনি দশজনে বলে ওঠেন, কি দ-নীতির কথা। বিষয়বধির মতে সৌন্দর্যপ্রিয়তা বিলাসিতা এবং রূপের চচা চরিত্রহীনতার পরিচয় দেয়। সন্দরের উপর এদেশে সত্যের অত্যাচার কম, কেননা এদেশে সত্যের আরাধনা করবার লোকও কম। শিবই হচ্ছে এখন আমাদের একমাত্র, কেননা অমনি-পাওয়া, ধন। এ তিনটির প্রতিটি যে প্রতিঅপরটির শত্র, তার কোনো প্রমাণ নেই। সুতরাং এদের একের প্রতি অভক্তি অপরের প্রতি ভক্তির পরিচায়ক নয়। সে যাই হোক, শিবের দোহাই দিয়ে কেউ কখনো সত্যকে চেপে রাখতে পারে নি; আমার বিশ্বাস, সুন্দরকেও পারবে না। যে জানে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, সে সে-সত্য স্বীকার করতে বাধ্য, এবং সামাজিক জীবনের উপর তার কি ফলাফল হবে সেকথা উপেক্ষা করে সে-সত্য প্রচার করতেও বাধ্য। কেননা, সত্যসেবকদের একটা বিশ্বাস আছে যে, সত্যজ্ঞানের শেষফল ভালো বই মন্দ নয়। তেমনি যার রূপজ্ঞান আছে, সে সৌন্দর্যের চর্চা এবং সুন্দর বস্তুর সৃষ্টি করতে বাধ্য তার আশু সামাজিক ফলাফল উপেক্ষা করে, কেননা রুপের পূজারীদেরও বিশ্বাস যে, রূপজ্ঞানের শেষফল ভালো বই মন্দ নয়। তবে মানুষের এ জ্ঞানলাভ করতে দেরি লাগে।
শিবজ্ঞান আসে সবচাইতে আগে। কেননা, মোটামুটি ও-জ্ঞান না থাকলে সমাজের সৃষ্টিই হয় না, রক্ষা হওয়া তো দুরের কথা। ও জ্ঞান বিষয়বৃদ্ধির উত্তমাঙ্গ হলেও একটা অঙ্গমাত্র।
তার পর আসে সত্যের জ্ঞান। এ জ্ঞান শিবজ্ঞানের চাইতে ঢের সক্ষমজ্ঞান এবং এ জ্ঞান আংশিকভাবে বৈষয়িক, অতএব জীবনের সহায়; এবং আংশিকভাবে তার বহির্ভূত, অতএব মনের সম্পদ।
সবশেষে আসে রূপজ্ঞান। কেননা, এ জ্ঞান অতিসক্ষম এবং সাংসারিক হিসেবে অকেজো। রূপজ্ঞানের প্রসাদে মানুষের মনের পরমায়ু বেড়ে যায়, দেহের নয়। সুনীতি সভ্যসমাজের গোড়ার কথা হলেও সুরুচি তার শেষকথা। শিব সমাজের ভিত্তি, আর সুন্দর তার অভ্রভেদী চড়া।
অবশ্য হার্বার্ট স্পেনসার বলেছেন যে, মানুষের রূপজ্ঞান আসে আগে এবং সত্যজ্ঞান তার পরে। তার কারণ, যে জ্ঞান তাঁর জন্মায় নি, তিনি মনে করতেন সে জ্ঞান বাতিল হয়ে গিয়েছে। সত্যকথা এই যে, মানবসমাজের পক্ষে রূপজ্ঞান লাভ করাই সাধনাসাপেক্ষ খোয়ানো সহজ। আমাদের পর্বপুরুষদের সাধনার সেই বঞ্চিত ধন আমরা অবহেলাক্রমে হারিয়ে বসেছি। বিলেতি সভ্যতার কেজো অংশের সংস্পর্শে আমাদের মনের ভিত টলকে আর না-টলুক, তার চড়া ভেঙে পড়েছে।
এবিষয়ে বৌদ্ধদর্শনের মত প্রণিধানযোগ্য। বৌদ্ধদার্শনিকেরা কল্পনা করেন যে, এ জগতে নানা লোক আছে। সবনীচে কামলোক, তার উপরে রূপলোক, তার উপরে ধ্যানলোক ইত্যাদি।
আমার ধারণা, আমরা-সব জন্মত কামলোকের অধিবাসী; সুতরাং রূপলোকে যাওয়ার অর্থ আত্মার পক্ষে ওঠা, নামা নয়।
আর-এক কথা, রূপের চর্চার বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, আমরা দরিদ্র জাতি–অতএব ও আমাদের সাধনার ধন নয়। এ ধারণার কারণ, ইউরোপের কমার্শিয়ালিজম, আমাদের মনের উপর এ যুগে রাজার মত প্রভুত্ব করছে। সত্যকথা এই যে, জাতীয়-শ্রীহীনতার কারণ অর্থের অভাব নয়, মনের দারিদ্র। তার প্রমাণ, আমাদের হালফ্যাশানের বেশভূষা সাজসজ্জা আচারঅনুষ্ঠানের শ্রীহীনতা সোনার-জলে ছাপানো বিয়ের কবিতার মত আমাদের ধনীসমাজেই বিশেষ করে ফুটে উঠেছে। আসল কথা, আমাদের নবশিক্ষার বৈজ্ঞানিক আলোক আমাদের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করুক আর নাই করুক, আমাদের রূপেকানা করেছে। গুণ হয়ে দোষ হল বিদ্যার বিদ্যায়’–ভারতচন্দ্রের একথা সুন্দরের দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে, আমাদের সকলের পক্ষেই সমান খাটে। আর যদি এইকথাই সত্য হয় যে, আমরা সুন্দরভাবে বাঁচতে পারি নে— তাহলে আমাদের সুন্দরভাবে মরাই শ্রেয়। তাতে পৃথিবীর কারও কোনো ক্ষতি হবে না, এমনকি আমাদেরও নয়।
ফাল্গুন ১৩২৩