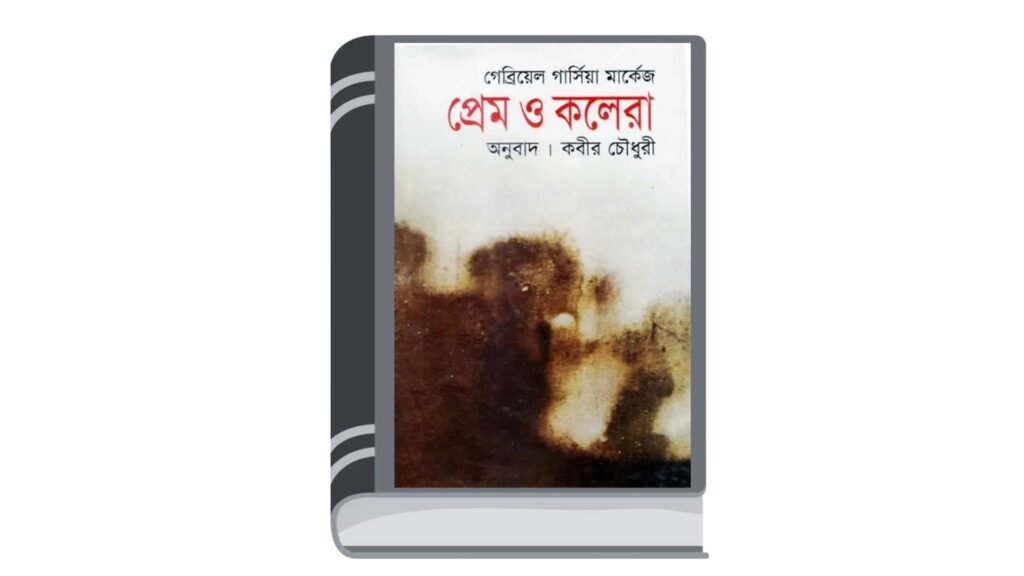প্রেম ও কলেরা – ১৪
১৪
ডাক্তার উরবিনো, বংশ গৌরব রক্ষায় সমর্পিত, স্ত্রীর অনুনয়-অনুরোধে কান দিলেন না, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ঈশ্বরের প্রজ্ঞায় এবং তার স্ত্রীর নিজেকে সব কিছুর সঙ্গে মানিয়ে নেবার অপরিসীম ক্ষমতায় সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এক সময়ে তাঁর যে-মায়ের ছিল জীবনের মধ্যে আনন্দ লাভের অনন্য ক্ষমতা, যিনি সব চাইতে সন্দিগ্ধ মানুষের মধ্যেও বাঁচার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলতে পারতেন, সেই মায়ের অবনতি- অবক্ষয় তাঁকে গভীর বেদনা দিল। তিনি ছিলেন সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, তাঁর সামাজিক পারিপার্শ্বিকতায় যে মানবিক অনুভূতিশীলতা দেখা যেতো না তাঁর মধ্যে তা উপস্থিত ছিল, চল্লিশ বছর ধরে তিনি তাঁর সামাজিক স্বর্গের প্রাণ ছিলেন, ছিলেন তার দেহ ও আত্মা। কিন্তু বৈধব্য তাঁকে তিক্ত করে তুলেছিল, তাঁকে দেখে মনে হত না যে তিনি সেই আগের মানুষ, এখন শিথিল, কটুভাষী, সারা দুনিয়ার শত্রু। তাঁর অবক্ষয়ের একমাত্র সম্ভাব্য কারণ ছিল স্বামীর প্রতি গভীর তিক্ততা, যিনি কৃষ্ণাঙ্গ জনতার জন্য জেনে শুনে আত্মাহুতি দেন, যখন তাঁর পক্ষে উপযুক্ত আত্মদান হত স্ত্রীর জন্য বেঁচে থাকা। সে যাই হোক, ফারমিনা ডাজার সুখী বিবাহ তাদের মধুচন্দ্রিমা পর্যন্তই স্থায়ী হয়। যে একমাত্র মানুষ তার চূড়ান্ত ধ্বংস প্রতিরোধে ফারমিনাকে সাহায্য করতে পারতেন তিনি তাঁর মায়ের শক্তিমত্তার সামনে ভয়ে পুরোপুরি অক্ষম হয়ে পড়েন। তার এই মরণ ফাঁদের জন্য ফারমিনা ডাজা তার নির্বোধ ননদদের নয়, তার অর্ধউন্মাদ শাশুড়িকে নয়, সে দায়ী করল তার স্বামীকে। বড় বেশি দেরিতে তার সন্দেহ হল যে- লোককে সে বিয়ে করেছে তাঁর পেশাগত কর্তৃত্ব ও জাগতিক মাধুর্যের আড়ালে তিনি আসলে একজন অতিশয় দুর্বল মানুষ, তাঁর ঐতিহ্যবাহী পারিবারিক বংশগৌরবের সামাজিক গুরুভারের চাপে সাহসী ভূমিকায় অবতীর্ণ একটা হতভাগা।
ফারমিনা তার নবজাত পুত্রের কাছে আশ্রয় নিল। সে যখন অনুভব করলো যে শিশুটি তার দেহ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তখন তার মধ্যে একটা নিজের নয় এমন একটা জিনিস তাকে ছেড়ে গেল। তারপর ধাত্রী তার গর্ভজাত সন্তান তার সামনে তুলে ধরলো, কাঁচা, চর্বি রক্ত মাখা, নাভির ফিতা গলায় জড়ানো, তাকে দেখে তার মনে বিন্দুমাত্র স্নেহ জেগে ওঠে নি। কিন্তু বিশাল বাড়িটিতে তার নিঃসঙ্গতার মধ্যে সে ওকে চিনতে শেখে, দুজনেই দুজনকে জানতে শেখে এবং গভীর আনন্দের সঙ্গে সে আবিষ্কার করে যে নিজের ছেলেমেয়ে বলেই কেউ তাদের ভালোবাসে না, তাদের লালনপালন করার সময় যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে সেজন্যই সে তাদের ভালোবাসে। তার এই দুর্ভাগ্যের সময়ে যা কিছু বা যে কাউকে সে তার ছেলের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পারতো না তাকেই সে ঘৃণা করতো। তার নিঃসঙ্গতা, সমাধি প্রাঙ্গনের বাগান, জানালাবিহীন বিশাল ঘরগুলিতে কোন রকমে সময় কাটানো এই সব তাকে বিষণ্ণ করে রাখতো। পাশের পাগলাগারদ থেকে উন্মাদিনীদের চিৎকার ভেসে আসতো, তার মনে হত সেও বুঝি পাগল হয়ে যাচ্ছে। রাত কাটতে চাইতো না। বাড়িতে এরা রোজ খাবার টেবিলে এম্ব্রয়ডারি করা টেবিল ক্লথের ওপর রুপার থালা-বাসন, কাঁটা চামচ ইত্যাদি সাড়ম্বরে সাজাতো, উপরে ঝুলতো ঝাড়বাতি, এসব দেখে তার খুব লজ্জা বোধ হত। টেবিলের চারপাশে বসে পাঁচজন ছায়ার মতো মানুষ কফি আর কেক খেতো। সন্ধ্যায় মালা জপ, খাবার টেবিলে সবার কৃত্রিম আচার-আচরণ, সে রুপার বাসন-চামচ-পাত্র কেমন করে ধরে তার নিরন্তর সমালোচনা, রাস্তার মেয়ের মতো তার হাঁটাচলা, সার্কাসের মেয়ের মতো তার কাপড়-জামা, এমনকি সে যে রকম গ্রাম্য ভঙ্গিতে স্বামীকে সম্বোধন করে আর বুকের ওপর কাপড় না টেনে দিয়ে সন্তানকে যেভাবে স্তন্যপান করায় তার নিন্দাবাদ তার মনকে ঘৃণায় পূর্ণ করে দিতো। সে যখন বিকাল পাঁচটার চা-য়ে তার প্রথম আমন্ত্রণ জানায় তখন সাম্প্রতিক বিলেতি ফ্যাশান অনুযায়ী পরিবেশিত হয় রাজকীয় ছোট ছোট কেক ও পুষ্পাকৃতির মিষ্টি, তারপর বাসি পনীর, চকোলেট আর গোল গোল কাসাভা রুটির পরিবর্তে সে যখন ওই বদ্ধ বাড়িতে ঘামের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য অন্য কিছু পরিবেশন করতে চাইলো তখন ডোনা ব্লাঙ্কা তাতে আপত্তি করলেন। তার স্বপ্নকেও তিনি রেহাই দিলেন না। একদিন সকালে ফারমিনা ডাজা তার গত রাতে দেখা একটা স্বপ্নের কথা বলে, সে দেখেছে বাড়ির ঘরগুলির ভেতর দিয়ে একজন নগ্নদেহ অপরিচিত মানুষ ছাই ছিটাতে ছিটাতে হেঁটে যাচ্ছে, এটুকু বলতেই ডোনা ব্লাঙ্কা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, ‘কোন ভদ্র মেয়ে এ ধরনের স্বপ্ন দেখে না।’
সব সময় অন্য একজনের বাড়িতে বাস করছে এই অনুভূতির সঙ্গে আরো দুটি বৃহত্তর দুর্ভাগ্য যুক্ত হল। একটা হল প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় বেগুন থাকতো, নানা পদের, নানা রকম রান্নার। ডোনা ব্লাঙ্কা তাঁর মৃত স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধার কারণে এর কোন ব্যত্যয় করতে রাজি হলেন না, আর ফারমিনাও কিছুতেই বেগুন খেতে রাজি হল না। ছেলেবেলা থেকেই সে বেগুনকে ঘেন্না করতো, মুখে দিয়ে দেখার আগে থেকেই, কারণ বেগুন দেখলেই তার মনে হত ওটা বিষের রঙ। কিন্তু এখন তার মনে হল ছেলেবেলার ওই ব্যাপারটা তার পরবর্তী জীবনের জন্য ভালোই হয়েছিল। পাঁচ বছর বয়সের সময় সে যখন বেগুনের সঙ্গে বিষের রঙের কথা বলেছিল তখন তার বাবা তাকে ছ’জনের জন্য রান্না করা এক পাত্র বেগুনের তরকারি জোর করে খাইয়েছিল। তখন তার মনে হয়েছিল সে বুঝি মরে যাচ্ছে, কারণ প্রথমে সে চূর্ণ চূর্ণ বেগুন বমি করে এবং পরে ওই শাস্তির প্রতিষেধক রূপে তাকে এক পেয়ালা ক্যাস্টার অয়েল পান করতে হয়। দুটি জিনিসই তার স্মৃতিতে একটি জোলাপ হয়ে তালগোল পাকিয়ে যায়, যেমন স্বাদের জন্য তেমনি বিষের ভয়ে। এখন মাই ডি কাসালডুয়েরোর প্রাসাদে খাবার টেবিলে তাকে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখতে হত, যেন ক্যাস্টর অয়েলের বরফশীতল বিবমিষা দিয়ে তাকে ওদের সহৃদয়তার মূল্য পরিশোধ করতে না হয়।
অন্য দুর্ভাগ্যটা ছিল একটা বীণা। একদিন, তিনি কী বোঝাতে চাইছেন সে সম্পর্কে বিশেষ সচেতন থেকে, ডোনা ব্লাঙ্কা বললেন, “যে মেয়ে পিয়ানো বাজাতে জানে না সে যে রুচিশীল এ আমি বিশ্বাস করি না।” কিন্তু তাঁর ওই নির্দেশ তাঁর পুত্রও মেনে নিতে পারে নি, কারণ পিয়ানো বাজানো শিখতে গিয়ে তাকে তার ছেলেবেলায় ক্রীতদাসের মতো দুঃসহ কষ্ট করতে হয়, যদিও বড়ো হয়ে তার জন্য তিনি কৃতজ্ঞই হন। কিন্তু তাঁর দৃঢ়চেতা পঁচিশ বৎসর বয়সের স্ত্রীকে যে ওই শাস্তি দেয়া যেতে পারে তা তিনি কল্পনাও করতে পারলেন না। তখন তিনি একটা শিশুসুলভ যুক্তি দিয়ে মায়ের কাছ থেকে একটা ছাড় আদায় করলেন। তিনি বললেন যে বীণা হচ্ছে দেবদূতদের যন্ত্র, আর তাই পিয়ানোর জায়গায় বীণা বহাল হল। ভিয়েনা থেকে একটি বীণা আনানো হল, দেখে মনে হল যেন সোনার বীণা, ধ্বনিও নির্গত হয় সোনার মতো, এক সময় এটা নগর জাদুঘরের সব চাইতে মূল্যবান উত্তরাধিকার সূত্রেপ্রাপ্ত বস্তুগুলির অন্যতম বলে বিবেচিত হয়, পরে একটা অগ্নিকাণ্ডে জাদুঘরের সব কিছুর সঙ্গে সেটাও ভস্মীভূত হয়ে যায়। চূড়ান্ত আত্মাহুতি দানের মাধ্যমে বিপর্যয় এড়ানোর প্রয়াসে ফারমিনা ডাজা ওই বিলাসবহুল কারাদণ্ড মাথা পেতে নিয়েছিল। মোমপক্স শহর থেকে আনীত এক প্রবীণ শিক্ষককুলের শিক্ষকের কাছ থেকে সে তালিম নিতে শুরু করে, কিন্তু তিনি দু’সপ্তাহ পরে আকস্মিক মৃত্যুপথে পতিত হন। এরপর ফারমিনা কয়েক বছর ধরে বিদ্যামন্দিরের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞদের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে, যদিও তাদের গোর-খোদকদের মতো শ্বাস-প্রশ্বাস তার বাদনের দ্রুত লয়কে প্রায়ই বিকৃত করে তুলতো।
তার বাধ্যতায় সে নিজেই অবাক হল। আসলে যদিও সে নিজের নিভৃততম চিন্তায় কিংবা একদা স্বামীর সঙ্গে প্রেম করার সময়ে পরিচালিত নীরব তর্ক-বিতর্কের সময় কখনো স্বীকার করে নি, তবুও সে অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে তার নতুন জগতের সামাজিক প্রথাসমূহ ও সংস্কারাবলীর জালে ধৃত হয়। প্রথম দিকে সে একটা আনুষ্ঠানিক উচ্চারণ দ্বারা তার নিজের চিন্তার স্বাধীনতা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করতো : “যখন হাওয়া দিচ্ছে তখন নিকুচি করি পাখার।” কিন্তু পরে, তার সযত্নে স্বোপার্জিত অধিকারগুলি সংরক্ষণের স্বার্থে এবং অন্যদের তাচ্ছিল্য কিংবা তাদের সামনে অপ্রস্তুত হওয়া থেকে রক্ষা পাবার জন্য সে নানা অপমান-অবহেলাও স্বেচ্ছায় মেনে নেয়, সে আশা করে যে ঈশ্বর শেষ পর্যন্ত ডোনা ব্লাঙ্কাকে করুণা করবেন, তিনি সারাক্ষণ তাঁর কাছে যে মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করেন ঈশ্বর তাঁর সে প্রার্থনা মঞ্জুর করবেন।
ডাক্তার উরবিনো তাঁর নিজের দুর্বলতার সমর্থনে নানা রাশভারি যুক্তির অবতারণা করতেন, সেগুলি চার্চের বিধানের পরপন্থী কিনা সে সম্পর্কেও তিনি নিজেকে প্রশ্ন করতেন না। স্ত্রীর সঙ্গে তার অসুবিধার মূলে যে এই গৃহের অতিপরিশ্রুত হাওয়া তা তিনি মানতে রাজি ছিলেন না। তিনি বরং তার দায়দায়িত্ব চাপাতেন বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটির প্রকৃতির মধ্যে। দুটি মানুষ যারা পরস্পরকে প্রায় চেনেই না, যাদের মধ্যে কোন যোগসূত্র নেই, যাদের চরিত্র আলাদা, বড় হবার পরিবেশ ভিন্ন রকম, এমনকি যাদের লিঙ্গ পর্যন্ত ভিন্ন, হঠাৎ তাদের একসঙ্গে ঘুমাতে হবে, তাদের অংশ নিতে হবে দুটি নিয়তিতে, ভাগ্য যেখানে সে-দুটিকে পরস্পরের উল্টো দিকে পরিচালিত করছে এটা সফল হবার কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি নাই। তিনি বলতেন, “বিয়ের সমস্যা হল প্রতি রাতে যৌন মিলনের পর তা শেষ হয়, তারপর প্রতি প্রভাতে প্রাতরাশের পূর্বে তাকে পুনর্নির্মিত করতেই হয়।” সব চাইতে ভয়ানক হল তাদের বিয়ে, যেখানে তারা দুজন উঠে এসেছে পরস্পরবিরোধী দুটি শ্রেণী থেকে, তার ওপর সেই শহরে যা এখনো ভাইসরয়দের প্রত্যাগমনের স্বপ্ন দেখে। তাদের একমাত্র বন্ধন হতে পারতো প্রেমের মতো অসম্ভব ও ভঙ্গুর একটা জিনিস, যদি তেমন কিছু থেকে থাকে, আর তাদের ক্ষেত্রে তারা যখন বিয়ে করে তখন তেমন কিছু ছিল না, আর তারা যখন সেটা আবিষ্কারের দোরগোড়ায় তখন নিয়তি তাদেরকে বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেবার চাইতে আর বেশি কিছু করলো না।
বীণা পর্বের সময় তাই ছিল তাদের জীবনের অবস্থা। এক এক সময় আকস্মিক মধুর যুগপৎ সংঘটন ঘটতো, ডাক্তার স্নান করছেন আর সে হঠাৎ বাথরুমে আসতো, বিষাক্ত বেগুন ও তাঁর মাথাখারাপ বোনদের এবং যে-মা তাদের জন্ম দিয়েছেন সেই মা-র নানা যুক্তিতর্ক সত্ত্বেও, ডাক্তারের মধ্যে তখনো যেটুকু ভালোবাসা ছিল তার জোরেই তিনি ওকে তার গায়ে সাবান ঘষে দিতে বলতেন। ইউরোপে তার মনে যে ভালোবাসা জন্মেছিল তার অবশিষ্ট যৎসামান্য যা ছিল তাই দিয়ে সে সাবান ঘষতো, উভয়েই স্মৃতিকে প্রশ্রয় দিতেন, ইচ্ছা না করেও কোমল হতেন, মুখে কিছু না বলেও পরস্পরকে কামনা করতেন, অবশেষে সুগন্ধি সাবানের ফেনার মধ্যে মেঝের উপরেই সঙ্গমে লিপ্ত হতেন, আর কাপড় কাচার ঘর থেকে দাসীদের কথা তাদের কানে ভেসে আসতো : “ওদের যে আর ছেলেপুলে হচ্ছে না তার কারণ একটাই, ওরা এখন সহবাস করছে না।” মাঝে মাঝে কোনো উদ্দাম উৎসব শেষে তাঁরা যখন বাড়ি ফিরে আসতেন তখন দরজার ওপাশে হামাগুড়ি দিয়ে বসে থাকা স্মৃতিবিধুরতা তার এক থাবার আঘাতে তাদের ধরাশায়ী করতো, আর তখন একটা অত্যাশ্চার্য বিস্ফোরণ ঘটতো, আর তখন তারা আবার তাঁদের মধুচন্দ্রিমার অনবদমিত প্রেমিক-প্রেমিকায় রূপান্তরিত হতেন।
কিন্তু ওই বিরল সময়গুলি ছাড়া বিছানায় যাবার সময় হলেই ওদের দুজনের একজন অপর জনের চাইতে বেশি ক্লান্ত বোধ করতো। ফারমিনা ডাজা বাথরুমে, কিছুই না করে, অনেকক্ষণ কাটাতো, তার সুরভিত কাগজে মুড়ে সিগারেট বানিয়ে চুপচাপ ধূমপান করতো, নিজের বাড়িতে স্বাধীন ও কিশোরী অবস্থায় যে রকম সান্ত্বনাদায়ক ভালোবাসায় ডুবে থাকতো সে রকম অনুভূতি জাগিয়ে তুলতো নিজের মধ্যে, তার নিজের দেহের সে-ই কর্ত্রী তখন। তা না হলে তার মাথা ধরেছে, কিংবা ভীষণ গরম, কিংবা ঘুমের ভান করতো সে, কিংবা তার আবার মাসিক হয়েছে, মাসিক আর মাসিক, সব সময়েই মাসিক এত বেশি যে স্বীকারোক্তি ছাড়াই নিজেকে ভারমুক্ত করে স্বস্তি লাভের উদ্দেশ্যে তিনি একদিন ক্লাসে সাহস করে বলেই ফেলেন যে দশ বছর বিবাহিত জীবনযাপনের পর মেয়েদের এক সপ্তাহে তিনবার পর্যন্ত ঋতুস্রাব হতে পারে।
দুর্ভাগ্যের পর দুর্ভাগ্য জমতে থাকে। ওই ভীষণ খারাপ বছরগুলিতে ফারমিনা ডাজাকে আরেকটা ব্যাপারের মুখোমুখি হতে হয়, আগে হোক বা পরে হোক যা তাকে হতেই হতো। তার পিতার অবিশ্বাস্য ও সর্বদাই রহস্যময় কাজ কারবারের পিছনে আসল সত্যটা কি? প্রাদেশিক গভর্নর একদিন আগে খবর দিয়ে ডাক্তার জুভেনালে উরবিনোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও তাঁকে তাঁর শ্বশুরের বাড়াবাড়ির কথা জানান। একটি বাক্যে তিনি তার সারটি তুলে ধরেন, “মানুষের বা ঈশ্বরের এমন কোন আইন নেই যে ওই লোক লঙ্ঘন করে নি।” তাঁর বেশ কিছু গুরুতর কাজ পরিচালিত হয়েছে তাঁর জামাতার মর্যাদা ও সুনামের ছত্রছায়ায়, তিনি বা তার স্ত্রী এসব বিষয়ের কিছুই জানতেন না এটা বিশ্বাস করা কঠিন। ডাক্তার উপলব্ধি করলেন যে এখন যে একমাত্র সম্মান রক্ষা করা দরকার সেটা তাঁর নিজের, কারণ এখনও একমাত্র সেটাই অক্ষুণ্ণ আছে, তাই তিনি তাঁর মর্যাদা ও সুনামের সবটুকু ওজন নিয়ে ব্যাপারটাতে হস্তক্ষেপ করলেন, এবং তাঁর নিজের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে কেলেঙ্কারিটা চাপা দিতে সক্ষম হলেন। প্রথম জাহাজেই লোরেঞ্জো ডাজা এদেশ ছেড়ে চলে গেলেন, আর কখনো তিনি ফিরে আসেন নি। তিনি তাঁর স্বদেশে এমন ভাবে ফিরে গেলেন যেন স্মৃতিবিধুরতার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য মানুষ যেমন মাঝে মাঝে বেড়াতে যায় সেই ভাবে সেখানে যাচ্ছেন। তার ওপর কোন জোর খাটাতে হয় নি। তিনি অবশ্য বার বার বলেছেন যে তিনি নির্দোষ, তাঁর জামাতাকে বিশ্বাস করাতে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন, বলেছেন যে তিনি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন। মেয়ের জন্য তিনি অশ্রু বিসর্জন করতে করতে বিদায় নেন, তাঁর নাতির জন্য কাঁদেন তিনি, সেই দেশটির জন্যও কাঁদেন যেখানে সন্দেহজনক কাজকর্মের মাধ্যমে তিনি স্বাধীন ও ধনী হন, ক্ষমাতাশালী হন এবং বিত্ত ও ক্ষমতার সাহায্যে তাঁর কন্যাকে এক চমৎকার সম্ভ্রান্ত মহিলা করে তোলেন। বুড়ো হয়ে অসুস্থ অবস্থায় তিনি বিদায় নেন, কিন্তু তারপরও তিনি অনেক দিন বেঁচে ছিলেন, তাঁর কুকীর্তির শিকাররা যা আশা করেছিল তার চাইতেও অনেক বেশি দিন। ফারমিনা ডাজা যখন তাঁর মৃত্যু সংবাদ পায় তখন সে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস চাপতে পারে নি, প্রশ্ন এড়াবার জন্য সে কোন রকম শোকের পোশাক পরে নি, কিন্তু বেশ ক’মাস পর্যন্ত সে বাথরুমের দরজা তালাবদ্ধ করে নির্বাক ক্ষোভে প্রচুর কেঁদেছে, নিঃশব্দে ধূমপান করেছে, কেন সে জানে না, যদিও আসলে সে অশ্রু বিসর্জন করেছে তাঁর কথা মনে করে।
ফারমিনা ও ডাক্তারের তখনকার অবস্থার সব চাইতে উদ্ভট দিক ছিল এই যে তাদের সর্বাপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক ওই সময়ে জনসমক্ষে তাদের দেখে মনে হত এমন সুখী তারা আর কখনো হয় নি। কারণ তাদের বিরুদ্ধে সামাজিক পরিবেশের যে গোপন বৈরী ধারা প্রবাহিত হচ্ছিল, ওই সমাজ তাদের মেনে নিতে পারছিল না, তারা ভিন্ন রকম, তারা আধুনিক, তারা ঐতিহ্যকে লঙ্ঘন করছে, ওই বৈরিতার বিরুদ্ধে ডাক্তার ও ফারমিনা এই সময়েই তাদের সব চাইতে বড় বিজয়গুলি অর্জন করছিলেন। ফারমিনা ডাজার পক্ষে এটা বেশ সহজ ছিল। তার নতুন জগতের জীবনে, অপরিচয়জনিত অনিশ্চয়তা কেটে যাবার পর, সে দেখলো যে তুচ্ছ আচার-অনুষ্ঠান ও বাঁধাধরা গতানুগতিক কথাবার্তার একটা অধিসঞ্চারী সিস্টেম ছাড়া ওটা আর কিছুই নয়, ওই সব দিয়ে এই সমাজে ওরা একে অন্যকে আনন্দ দেয় যেন একে অন্যকে তাদের খুন করতে না হয়। প্রাদেশিক ওই লঘুচিত্ততার প্রধান লক্ষণ ছিল অজানার ভীতি। ফারমিনা আরো সরল ভাবে ব্যাপারটা সংজ্ঞায়িত করে : “জনজীবনের সমস্যা হল আতঙ্ক জয় করার শিক্ষালাভ করা, আর বিবাহিত জীবনের সমস্যা হল একঘেয়েমি জয় করার শিক্ষালাভ করা।” একটা অলৌকিক প্রকাশের স্বচ্ছতা নিয়ে সে অকস্মাৎ এই সত্যটি আবিষ্কার করে। সোশ্যাল ক্লাবের বিশাল সালোঁতে প্রবেশ করছিল সে, তার নববধূর দীর্ঘ পোশাকের পিছনের অংশ মাটিতে লুটাচ্ছে, ঘরের ভেতর অজস্র ফুলের মিশ্র গন্ধে বাতাস হাল্কা, সেখানে ওয়ালটজের ঔজ্জ্বল্য, ঘর্মাক্ত কলেবর, ভদ্রলোকদের হৈ চৈ, কেঁপে কেঁপে ওঠা রমণীরা তাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, বাইরের জগত থেকে এই যে ঝলমলে হুমকি তাদের মধ্যে এসে পড়লো কোন মন্ত্ৰ দ্বারা তারা এটা দূরীভূত করবে সেকথা ভাবছে, আর তখনই সত্যটা ফারমিনার চোখে ধরা পড়ে। সবে মাত্র তার একুশ বছর পূর্ণ হয়েছে, স্কুলে যাওয়া ছাড়া বাড়ির বাইরে যায় নি বললেই চলে, কিন্তু চারদিকে এক নজর তাকিয়েই সে বুঝলো যে তার প্রতিদ্বন্দ্বীরা তার প্রতি ঘৃণায় আলোড়িত নয়, তারা ভয়ে হতবুদ্ধি ও জড়তাপ্রাপ্ত। ওদের আরো বেশি ভয় পাইয়ে দেবার পরিবর্তে, যা সে ইতিমধ্যেই করছিল, সে ওদের প্রতি অনুকম্পা বশত নিজেকে চিনতে ওদের শেখাতে চাইলো। সে ওদের যেমন চেয়েছে ওরা তার চাইতে ভিন্ন রকম কিছু ছিল না, ঠিক শহরগুলির মতোই, ভালোও নয় খারাপও নয়, মনের মধ্যে সে এগুলি যেমন বানিয়ে নিয়েছে ঠিক তেমনই।
বিরতিহীন বৃষ্টি, বাজে ব্যবসায়ী, ঘোড়ার গাড়ির কোচোয়ানদের হোমারীয় স্থূলতা সত্ত্বেও সে পারীকে মনে রাখবে পৃথিবীর সব চাইতে নগরী নারী রূপে, সেটা কি ছিল বা ছিল না সেজন্য নয়, এই জন্য যে সেটা ছিল তার সব চাইতে সুখী সময়ের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। আর ডাক্তার উরবিনো তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত ওদের অস্ত্র দিয়েই ওদের শ্রদ্ধা আদায় করে নিতেন, শুধু তিনি ওই সব অস্ত্র প্রয়োগ করতেন অধিকতর বুদ্ধিমত্তা ও খুব হিসেব করা গাম্ভীর্যের সঙ্গে। এই দম্পতি ছাড়া এখানে কিছুই হত না। নাগরিক প্রদর্শনী, কবিতা উৎসব, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কোন পরহিতকর কাজের জন্য লটারির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ, দেশপ্রেমমূলক অনুষ্ঠান, প্রথম বেলুনে ভ্রমণ— ওঁদের ছাড়া কিছুই হত না। সব উদ্যোগেই প্রায় সব সময়ই ওঁরাই ছিলেন গোড়া থেকে এবং সর্বাগ্রে। ওই দুর্ভাগ্যপীড়িত সময়ে কেউই তাঁদের চাইতে বেশি সুখী কাউকে কল্পনা করতে পারতো না, তাদের চাইতে বেশি মধুর মিল বিশিষ্ট কোন বিয়ে হতে পারে বলে তারা মনে করতো না।
পারিবারিক প্রাসাদের শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ থেকে ফারমিনা ডাজা স্বস্তির আশ্রয় পেতো তার নিজের বাড়িতে, যে বাড়ি তার বাবা তাঁকে দিয়ে গিয়েছিলেন। লোকজনের দৃষ্টি থেকে পালাতে পারলেই সে সংগোপনে ইভাঞ্জেল পার্কে চলে যেতো, কিছু নতুন বন্ধু ও তার স্কুল ও ছবি আঁকার সময়ের পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতো : বিশ্বাসভঙ্গের একটা নিষ্পাপ বিকল্প। একক মা হিসাবে সে ঝঞ্ঝাটবিহীন প্রশান্ত সময় কাটাতো ওই বাড়িতে, তার বালিকা বয়সের যে সব স্মৃতি তখনো অবশিষ্ট ছিল তাকে সে নিজের চারপাশে জড়িয়ে রাখতো। সুরভিত কাকের বদলে সে রাস্তার বিড়াল তুলে এনে গালা প্লাসিডিয়ার তত্ত্বাবধানে সমর্পণ করলো। গালা প্লাসিডিয়া বুড়ো হয়ে গেছে, বাতের আক্রমণে আগের মতো দ্রুত নড়াচড়া করতে পারে না, তবু বাড়িটাতে আবার জীবনের স্পন্দন ফিরিয়ে আনতে সে ছিল তৎপর ও ইচ্ছুক। যে সেলাই ঘরে ফ্লোরেন্টিনো আরিজা ফারমিনা ডাজাকে প্রথম দেখে, যেখানে ডাক্তার উরবিনোর নির্দেশে তাকে তার জিভ বের করে দেখাতে হয় যেন তিনি সেখানে তার হৃদয়ের লেখা পড়তে পারেন, ফারমিনা ডাজা সে ঘর খুলে দেয়, সে তাকে রূপান্তরিত করে অতীতের এক পবিত্র পীঠস্থানে। একদিন শীতের এক অপরাহ্নে প্রবল ঝড় আসার উপক্রম হলে সে বারান্দার জানালা বন্ধ করতে গেলে ছোট্ট পার্কের বাদাম গাছের নিচে তার বেঞ্চে ফ্লোরেন্টিনো আরিজাকে বসে থাকতে দেখতে পায়, সে তার বাবার স্যুট পরে আছে, গায়ে ঠিক হবার জন্য সেটা বদল করা হয়েছে, কোলের ওপর তার বইটি খোলা অবস্থায় ধরা, কিন্তু ফারমিনা বিভিন্ন সময়ে ঘটনাচক্রে তাকে যে রকম দেখেছিল এখন তাকে সে রকম দেখলো না, তার স্মৃতিতে ফ্লোরেন্টিনোর যে ছবি আঁকা ছিল তার ওই বয়সের রূপটিই সে দেখলো। তার মনে হল স্বপ্নের মতো ওই ছবি বোধ হয় মৃত্যুর অশুভ সঙ্কেত। তার হৃদয় শোকে বিহ্বল হল। সে সাহস করে নিজেকে বললো, বোধ হয় ওর সঙ্গেই সে বেশি সুখী হত, তাকে ভালোবেসে, তার জন্য, সে ওর নিজের যে বাড়ির সংস্কার করেছিল ওকে নিয়ে সে একা ওই বাড়িতেই আসল সুখের সন্ধান পেতো, আর এই সরল উপপ্রমেয়টি তাকে হতাশায় নিমজ্জিত করলো, কারণ সে যে কী চরম অসুখী তা সে এর মধ্য দিয়েই উপলব্ধি করলো। তখন সে তার শক্তির শেষ বিন্দু জড়ো করে তার স্বামীকে, কোন রকম পাশ না কাটিয়ে, সরাসরি, তার সঙ্গে কথা বলতে বাধ্য করলো, তার মুখোমুখি হয়ে তার সঙ্গে তর্ক করতে বাধ্য করলো, যে-স্বর্গ সে হারিয়েছে তার জন্য সে ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ চিত্তে অশ্রু বিসর্জন করলো, শেষ মোরগের ডাক পর্যন্ত এসব চলতে থাকলো, তারপর এক সময় তাদের রাজকীয় ভবনের লেস-এর পর্দার ভেতর দিয়ে প্রভাতের আলো ঘরে ঢুকলো, সূর্য উঠলো, তার স্বামী এতো কথার ভারে, অনিদ্রায় চরম ক্লান্ত হয়ে, স্ত্রীর অঝোর চোখের জল থেকে শক্তি সংগ্রহ করে তাঁর জুতার ফিতা বাঁধলেন, কোমরের বেল্ট আঁট করলেন, তাঁর পৌরুষের যেটুকু তাঁর মধ্যে অবশিষ্ট ছিল তা নিজের মধ্যে সংহত করে নিলেন, তারপর স্ত্রীকে বললেন, হ্যাঁ, প্রিয়ে, আমরা ইউরোপে যে ভালোবাসা হারিয়ে রেখে এসেছিলাম আবার আমরা দুজনে মিলে তার খোঁজ করবো, আগামীকাল থেকেই সেটা শুরু হবে এবং সেটা চলবে অনাদিকাল পর্যন্ত। তাঁর সিদ্ধান্ত এতই প্রবল ছিল যে তিনি তাঁর যাবতীয় সম্পত্তির ব্যবস্থাপক ট্রেজারি ব্যাংকের সঙ্গে স্থির করে নিলেন, ওরা অবিলম্বে তাঁর বিশাল পারিবারিক সম্পদের হিসাব মিটিয়ে দেবে, শুরু থেকেই যা ছিল ছড়ানো-ছিটানো, বিভিন্ন ব্যবসায়ে, বিনিয়োগে, স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি, নানা চুক্তিতে, লোককাহিনীতে যা যতোটা বিশাল বিবেচনা করা হত তিনি জানতেন যে তা আসলে তত বিশাল নয়, তবুও এত বিশাল যে তা নিয়ে ভাবনার কোন দরকার পড়ে না। তিনি তাঁর সব সম্পদ সিলমোহর করা সোনায় রূপান্তরিত করলেন, অল্প অল্প করে তিনি তা তাঁর বিদেশী ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বিনিয়োগ করবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর এই রূঢ় নিষ্ঠুর দেশে নিজের বলতে আর কিছুই থাকবে না, এমনকি কবর দেয়ার জন্য এক টুকরা জমিও না।
ওদিকে ফারমিনা ডাজা যাই বিশ্বাস করার সিদ্ধান্ত নিক না কেন ফ্লোরেন্টিনোর অস্তিত্ব যথার্থই বিদ্যমান ছিল। ফারমিনাদের ফরাসি সামুদ্রিক জাহাজ যখন যাত্রার জন্য বন্দরে দাঁড়িয়েছিল তখন সে জাহাজ ঘাটে উপস্থিত ছিল, স্বামী-পুত্রসহ সোনালি রঙের ঘোড়াটানা গাড়িতে সে তাকে উঠতে দেখে, সেখান থেকে নামতে দেখে, বিভিন্ন সর্বজনীন উৎসব-অনুষ্ঠানে যেমন সে বহুবার দেখেছে ঠিক তেমনি একেবারে নিখুঁত। ওরা ওদের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিল, বড় হয়ে সে কেমন হবে এখনই তার চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল, সে হয়েও ছিল তাই। জুভেনাল উরবিনো তাঁর মাথার টুপি উঁচু করে ফ্লোরেন্টিনো আরিজাকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বলেছিলেন, ফ্ল্যান্ডার্স জয় করতে চললাম আমরা। ফারমিনা ডাজা তার মাথা নেড়েছিল, আর ফ্লোরেন্টিনো আরিজা তার টুপি খুলে মাথা ঈষৎ নুইয়ে প্রত্যাভিবাদন জানিয়েছিল। অকালে যে তার মাথায় টাকের আক্রমণ হচ্ছে তার জন্য বিন্দুমাত্র অনুকম্পা বোধ না করে ফারমিনা ডাজা তাকে লক্ষ করেছিল। ওই যে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে সে সর্বদা যেমন দেখেছে ঠিক তেমনি, কখনোই দেখে নি এমন একজনের ছায়া মাত্র।
ফ্লোরেন্টিনো আরিজার জন্যও এই সময়টা তার সর্বোত্তম সময়ের একটি ছিল না। তার কাজের চাপ দিন দিন বাড়ছিল, তীব্র হচ্ছিল, গোপন শিকার পর্বের মধ্যে একটা একঘেয়েমি দেখা যাচ্ছিল, সময় কাটছিল নিস্তরঙ্গ নিষ্প্রাণতার মধ্যে, আর এর মধ্যে দেখা দিল ট্রান্সিটো আরিজার চূড়ান্ত সঙ্কট, সম্পূর্ণ স্মৃতিবিস্তৃত, একেবারে ফাঁকা, ব্যাপারটা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যেখানে তিনি ফ্লোরেন্টিনো আরিজা সব সময় যে আরাম কেদারায় বসে কাগজ বা বই পড়তো সে দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে বলে উঠতেন, ‘তুমি কার ছেলে গো?’ ফ্লোরেন্টিনো সব সময় সত্য উত্তরটিই দিতো কিন্তু তিনি ওকে বাধা দিয়ে বিন্দুমাত্র দেরি না করে আবার বলতেন, ‘এবার একটা কথা বলো দেখি, বাছা, আমি কে?’
ভীষণ মোটা হয়ে গিয়েছিলেন তিনি, প্রায় নড়তেই পারতেন না, সারাটা সময় কাটাতেন টুকিটাকির দোকানে, যদিও বিক্রি করাবার মতো সেখানে আর কিছুই ছিল না। সকালে মোরগের প্রথম ডাকের সঙ্গে তিনি উঠে পড়তেন, সাজগোজ করতেন, পরের দিন ভোর না হওয়া পর্যন্ত তিনি এসব নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন, রাতে তিনি ঘুমাতেন না বললেই চলে। মাথায় ফুলের মালা জড়িয়ে, ঠোঁটে রঙ লাগিয়ে, মুখে আর বাহুতে পাউডার মেখে যার সঙ্গে তাঁর দেখা হত তাকেই জিজ্ঞাসা করতেন, “এখন বলো তো আমি কে?” প্রতিবেশীরা জানতো যে তিনি সর্বদা একটি উত্তরই প্রত্যাশা করতেন, “আপনি হচ্ছেন ছোট্ট রোশি মার্টিনেজ।” ছোটদের গল্পের বই থেকে এই চরিত্রটি তিনি চুরি করেছিলেন এবং শুধু ওই উত্তরেই তিনি সন্তুষ্ট হতেন। তিনি চেয়ারে বসে দুলতেন, লম্বা গোলাপি পালকের পাখা দিয়ে হাওয়া খেতেন, তারপর এক সময় আবার গোড়া থেকে শুরু করতেন : মাথায় কাগজের ফুলের মালা, চোখের পাতায় বেগুনি রঙ, ঠোঁটে লাল, মুখে মড়ার মতো সাদা রঙ, তারপর যাকে কাছে পেতেন তাকেই জিজ্ঞাসা করতেন, “এখন আমি কে?” তিনি যখন পাড়ার সার্বক্ষণিক হাস্যকৌতুকের পাত্র হয়ে উঠলেন তখন এক রাতে ফ্লোরেন্টিনো আরিজা পুরনো টুকিটাকি দোকনটার কাউন্টার ও জিনিসপত্র রাখার দেরাজগুলি টুকরা টুকরা করে খুলে ফেললো, রাস্তার দিকের দরজাটা পাকাপাকি ভাবে বন্ধ করে দিল, তারপর যে জায়গাটা পাওয়া গেল সেখানে মাকে রোশি মার্টিনেজের শোবার ঘরের যে বর্ণনা দিতে সে শুনেছে সে-বর্ণনা অনুযায়ী একটা ঘর সাজিয়ে দিল। এর পর থেকে তিনি আর কখনো জিজ্ঞাসা করেন নি তিনি কে।
কাকা দ্বাদশ লিওর পরামর্শে মায়ের দেখাশোনার জন্য ফ্লোরেন্টিনো আরিজা এক বয়স্কা মহিলাকে নিযুক্ত করে, কিন্তু ও বেচারী জেগে থাকার চাইতে বেশির ভাগ সময় ঘুমিয়েই কাটাতো, তা ছাড়া মাঝে মাঝে মনে হতো সে যে কে তা বোধ হয় সেও ভুলে গেছে। ফলে অফিস থেকে ফিরে মাকে ঘুম না পাড়ানো পর্যন্ত সে বাড়িতেই থাকতে লাগলো। কমার্শিয়াল ক্লাবে সে আর ডোমিনো খেলতে যেতো না। যে সব মেয়ে বন্ধুদের ওখানে যেতো তাদের কাছেও অনেক দিন ধরে আর যায় না। কারণ, অলিম্পিয়া জুলেটার সঙ্গে তার ভয়ঙ্কর সাক্ষাতের পর তার মধ্যে একটা বড় পরিবর্তন ঘটে।
তার মনে হল সে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছে। ফ্লোরেন্টিনো আরিজা সেদিন কাকা দ্বাদশ লিওকে সবেমাত্র বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে। অক্টোবর মাস, ভীষণ ঝড় শুরু হল, যে রকম ঝড় মাথা ঘুরিয়ে দেয়। ফ্লোরেন্টিনো আরিজা তার গাড়ির ভেতর থেকে একটি খুব চটপটে ক্ষীণাঙ্গী মেয়েকে দেখলো, তার পরনে কুচি দেয়া অরগাঞ্জার পোশাক, নববধূর গাউনের মতো। মেয়েটি ভীষণ ভয় পেয়ে রাস্তার এপাশ থেকে ওপাশে ছুটে যাচ্ছে, হাওয়া ওর ছাতা উড়িয়ে নিয়ে গেছে, ওটা ছুটে চলেছে সমুদ্রের দিকে। সে মেয়েটিকে গাড়িতে তুলে নিয়ে নিজের পথ ছেড়ে ঘুরে গিয়ে তাকে তার বাড়িতে নামিয়ে দিল। ওদের বাড়িটা ছিল একটা পুরনো রূপান্তরিত আশ্রম। সামনেই সমুদ্র, রাস্তা থেকে বারান্দাটা দেখা যায়, সেখানে অনেকগুলি পায়রার খাঁচা। পথে আসতে আসতে ও ফ্লোরেন্টিনোকে জানায় যে তার বিয়ে হয়েছে এখনও এক বছর পুরো হয় নি, স্বামী বাজারে ছোট ছোট মনোহারী সামগ্রী বিক্রি করে। ফ্লোরেন্টিনো আরিজা তাকে তার কোম্পানির জাহাজে অনেকবার দেখেছে, বিক্রির জন্য নানা জিনিসপাতি বোঝাই বাক্স জাহাজ থেকে নামাচ্ছে, আর বেতের একটা ঝুড়িতে এক গাদা পায়রা। নৌযানে চলাচলের সময় অনেক মা তাদের বাচ্চাদের বহন করার জন্য ওই রকম ঝুড়ি ব্যবহার করে। অলিম্পিয়া জুলেটাকে দেখে মনে হল সে বোলতা গোত্রভুক্ত, শুধু তার উঁচু নিতম্ব ও ক্ষুদ্র বক্ষের জন্যই নয়, তার তামার তারের মতো চুল, মুখের দাগ, গোল গোল প্রাণবন্ত সাধারণের চাইতে বেশি দূরত্বে স্থাপিত দুটি চোখ, তার সুরেলা কণ্ঠস্বর, সব কিছুই ছিল বোলতার মতো। আর তার ওই সুরেলা গলার কথাবার্তা ছিল বুদ্ধিদীপ্ত ও মজাদার। ফ্লোরেন্টিনো আরিজার মনে হল সে যতখানি আকর্ষণীয় তার চাইতে বেশি রসালো। ওকে তার বাড়িতে নামিয়ে দেবার পর পরই ফ্লোরেন্টিনো তার কথা ভুলে যায়। তার বাড়িতে সে বাস করতো তার স্বামী, স্বামীর বাবা এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের নিয়ে।
কয়েক দিন পর ফ্লোরেন্টিনো আরিজা ওর স্বামীকে বন্দরে দেখতে পায়, মাল নামাবার পরিবর্তে সে তখন জাহাজে মাল তুলছিলো, জাহাজ নোঙর ওঠাবার সঙ্গে সঙ্গে সে তার কানে অত্যন্ত স্পষ্ট শয়তানের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো। সে দিন অপরাহ্নে, কাকা দ্বাদশ লিওকে তাঁর বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে সে যেন দৈবযোগে অলিম্পিয়া জুলেটার বাসভবনের সামনে দিয়ে গেল। সে তাকে দেখতে পেলো বেড়ার ওপাশে, কলকল করা পায়রাগুলিকে খাওয়াচ্ছে। গাড়ি থেকেই ফ্লোরেন্টিনো তাকে উদ্দেশ করে জিজ্ঞাসা করলো, “কত দাম একটা পায়রার?” ও তাকে চিনতে পারলো, হাসিমাখা গলায় উত্তর দিলো, “এগুলি বিক্রির জন্য নয়।” ফ্লোরেন্টিনো বললো, “তা হলে একটা পেতে হলে আমাকে কি করতে হবে?” পায়রাগুলিকে খাওয়াতে খাওয়াতেই ও জবাব দিল, “হারিয়ে যাওয়া ওকে ঝড়ের মধ্যে পেলে তাকে গাড়ি করে তার খাঁচায় ফিরিয়ে দিতে হবে আপনাকে।” সেদিন ফ্লোরেন্টিনো বাড়িতে ফিরে এলো অলিম্পিয়ায় কাছ থেকে একটা ধন্যবাদ-উপহার নিয়ে : একটা পত্রবাহক পায়রা, পায়ে ধাতুর আংটি পরানো।
পরের দিন বিকালে, ঠিক রাতের খাবার সময়, পায়রা-প্রেমিক উপহার দেয়া পত্রবাহক পায়রাটিকে তার খোপের কাছে দেখতে পেলো। সে প্রথমে ভেবেছিলো ওটা বুঝি পালিয়ে এসেছে, কিন্তু পরে আংটির মধ্যে এক টুকরা কাগজ দেখলো সে, ভালোবাসার ঘোষণা। এই প্রথম ফ্লোরেন্টিনো আরিজা এসব কাজের একটা লিখিত চিহ্ন রাখলো, তবে নাম সই না করার মতো বিবেচনা বোধ সে দেখিয়েছিল। পর দিন বিকালে সে যখন বাড়িতে ঢুকছিল, সেটা ছিল বুধবার, একটা রাস্তার ছেলে খাঁচায় পোরা আগের পায়রাটি তার হাতে দিয়ে তাকে একটা মুখস্থ করা বার্তা দিল, পায়রা- মহিলা আপনাকে এটা পাঠাচ্ছেন, পায়রাটা যেন আবার পালিয়ে যেতে না পারে সেজন্য তিনি আপনাকে খাঁচা তালাবদ্ধ করে রাখতে বলেছেন, তিনি শেষ বারের মতো এটা ফেরত পাঠাচ্ছেন আর পাঠাবেন না। এটাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবে ফ্লোরেন্টিনো ভেবে পেলো না : হয় পায়রাটা তার ওড়ার পথে চিঠি হারিয়ে ফেলেছে, নয় তো পায়রার মালিক সাধু সেজে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কিংবা ও পায়রাটা তার কাছে পাঠিয়েছে সে যেন আবার ওটা ওকে ফেরৎ পাঠাতে পারে। তবে পায়রার সঙ্গে একটা উত্তর পাঠালে ব্যাপারটা স্বাভাবিক হতো।
অনেক চিন্তা ভাবনার পর শনিবার সকালে আরেকটা সইবিহীন চিঠি দিয়ে ফ্লোরেন্টিনো আরিজা আবার পায়রাটা ফেরত পাঠালো। এবার তাকে পরের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল না। সেদিন বিকালে ওই একই বালক আরেকটা খাঁচায় করে পায়রাটা ফেরত নিয়ে এলো, সঙ্গে আনলো একটা বার্তা, পায়রাটা আবার পালিয়ে গিয়েছিল তাই তিনি এবারও ওটা ফেরত পাঠাচ্ছেন, পরশু সেটা ফেরত দিয়েছেন করুণার বশবর্তী হয়ে, কিন্তু আরেকবার যদি ওটা পালিয়ে যায় তা হলে সত্যিই তিনি আর ওটা ফেরত পাঠাবেন না। ট্রান্সিটো আরিজা অনেক রাত পর্যন্ত পায়রাটাকে নিয়ে খেলা করেন, খাঁচা থেকে ওটাকে বের করে বুকের কাছে ধরে বাচ্চাদের ঘুম পাড়ানি গান শুনিয়ে ওকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করেন, আর তখন ফ্লোরেন্টিনো আরিজা লক্ষ করে যে তার পায়ের আংটির মধ্যে একটা ছোট্ট কাজের টুকরা লাগানো আছে, সেখানে মাত্র একটা লাইন লেখা রয়েছে : ‘আমি কোনো বেনামী চিঠি গ্রহণ করি না। ফ্লোরেন্টিনো আরিজা লেখাটা পড়লো, তার হৃদয় আনন্দে তোলাপাড় করে উঠলো, যেন এটা তার প্রথম অভিযানের চূড়ান্ত সার্থক পরিণতি। সে রাতে ফ্লোরেন্টিনো এক ফোঁটা ঘুমালো না, অধৈর্য হয়ে সারা রাত সে বিছানায় এপাশ ওপাশ করে। পরদিন খুব ভোরে, আপিসে যাবার আগে, সে আবার পায়রাটা ছেড়ে দিল, সঙ্গে দিল একটা প্রেমপত্র, এবার তার স্পষ্ট সইসহ। তাছাড়া সে আংটার মধ্যে গুঁজে দিল তার বাগানের সব চাইতে তাজা, সব চাইতে লাল, সব চাইতে সুগন্ধী গোলাপটা।
কিন্তু ব্যাপারটা খুব সহজ হয় নি। তিন মাস পশ্চাদ্ধাবনের পরও পায়রা-প্রেমিক মহিলা একই উত্তর পাঠাতে থাকে : ‘আমি ওই সব মেয়েদের মতো নই।’ কিন্তু সে ফ্লোরেন্টিনোর বার্তা গ্রহণ করতে কখনো অস্বীকৃতি জানায় নি, আকস্মিক ঘটনাচক্রের মতো করে ফ্লোরেন্টিনো ওর সঙ্গে সাক্ষাতের যেসব ব্যবস্থা করতো তাও সে রক্ষা করতো। ফ্লোরেন্টিনো আরিজা এখন একেবারে এক ভিন্ন মানুষ। যে-প্রেমিক কখনো তার মুখ দেখাতো না, যে লোক ভালোবাসা পাবার জন্য ছিল চরম ব্যগ্র অথচ দেবার বেলায় ভীষণ কৃপণ, যে তার কোনো প্রেয়সীর ভালোবাসার ছাপই তার হৃদয়ে কখনো পড়তে দেয় নি, যে সব সময়ই ছিল অতর্কিত আক্রমণের জন্য ওঁৎ পেতে থাকা এক শিকারি- এখন সে প্রকাশ্য রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, আনন্দউচ্ছল সই করা প্রেমপত্র লিখছে, দুঃসাহসিক উপহার সামগ্রী পাঠাচ্ছে, পায়রা-প্রেমিকের বাড়ির সামনে অবিবেচকের মতো রাতভর দাঁড়িয়ে থাকছে, এমন কি দুবার সে এই কাজটি করেছে যখন মহিলার স্বামী শহরের বাইরে বা বাজারে যান নি। তার একেবারে অল্প বয়সের পর এই প্রথম তার মনে হল যে প্রেমের বর্শা তাকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলেছে।
তাদের প্রথম সাক্ষাতের ছয় মাস পর, অবশেষে, তারা নির্জনে মিলিত হবার সুযোগ পেলো। জাহাজঘাটে একটা নৌযানে রঙ লাগানো হচ্ছিল। তার একটা ক্যাবিনে ওরা দুজন মিলিত হল। সেটা ছিল এক বিস্ময়কর অপরাহ্। অলিম্পিয়া জুলেটা এক চমকিত পায়রা-প্রেমিকের সানন্দ ভালোবাসার অনুভূতি লাভ করলো, একটা গভীর প্রশান্তিতে তার দেহ-মন ভরে যায়, দেহ সম্ভোগের চাইতে ওই প্রশান্তি সে কম উপভোগ করে নি। সে ওই শ্লথগতি প্রশান্তির মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নগ্ন অবস্থায় কাটিয়ে দিল। ক্যাবিনটা খুলে ফেলা হয়েছিল, অর্ধেকটা রঙ করা হয়ে গেছে। ওরা দুজন এখান থেকে একটা সুখী বিকালের স্মৃতির সঙ্গে নিয়ে যাবে তারপিন তেলের গন্ধও। একটা আকস্মিক অনুপ্রেরণায় ফ্লোরেন্টিনো আরিজা হাতের কাছে পাওয়া একটা লাল রঙের টিন খুলে তার ভেতরে নিজের তর্জনী ডুবিয়ে সুন্দরী পায়রা-প্রেমিকের তলপেটের নিম্নাংশে দক্ষিণে মুখ করা একটা রক্তের তীর এঁকে দিল, তারপর ওই রঙ দিয়েই লিখলো, “এই বিল্লীটা আমার।’ সেদিন রাতে অলিম্পিয়া জুলেটা ওর স্বামীর সামনে নিজের জামা-কাপড় খুললো, তার গায়ের লেখার কথা সে ভুলেই গিয়েছিল, স্বামী একটি কথাও বললো না, তার শ্বাস-প্রশ্বাসে পর্যন্ত কোন পরিবর্তন দেখা গেল না, অলিম্পিয়া যখন ওর রাত- কামিজ পরছিল তখন সে বাথরুমে ঢুকে তার ক্ষুরটা নিয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো, তারপর এক পোঁচে ওর গলাটা কেটে ফেললো।
অনেক দিন পর পলাতক স্বামী যখন ধরা পড়ে শুধু তখনই ফ্লোরেন্টিনো বিষয়টা জানতে পারে। স্বামী খবরের কাগজকে তার অপরাধের কারণটা জানায়, এও বলে যে সে-ই হত্যা করেছে। তার সই করা চিঠির কথা ভেবে ফ্লোরেন্টিনো আরিজা বহু বছর প্রচণ্ড আতঙ্কের মধ্যে কাটায়, খুনির কারাবাসের সময়সূচির প্রতি নজর রাখে সে, তবে তারও গলা কাটা যেতে পারে সেই ভয়ে ততটা নয়, জনসাধারণের মধ্যে তার সম্পর্কে যে কলঙ্ক ছড়িয়ে পড়বে তার জন্যও ততটা নয়, যতটা তার বিশ্বাস ভঙ্গের কথা জেনে ফারমিনা ডাজা কি ভাববে সেই কথা চিন্তা করে।
তার অপেক্ষমান বছরগুলির একটি দিনে যে-মহিলা তার মায়ের দেখাশোনা করতো সে হঠাৎ অসময়ে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে বাজারে প্রত্যাশিত সময়ের চাইতে বেশিক্ষণের জন্য আটকা পড়ে যায়। বাড়িতে এসে সে ট্রান্সিটো আরিজাকে তাঁর দোল-চেয়ারে বসে থাকতে দেখলো, সব সময়ের মতো গালে-ঠোঁটে রঙ মাখানো, সাজসজ্জা করা, চোখ দুটি অসম্ভব উজ্জ্বল, মুখে একটা দুষ্টুমির হাসি, দু’ঘণ্টা পার হয়ে যাবার আগে তাঁর দেখা-শোনা করার মহিলা বুঝতেই পারে নি যে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। মৃত্যুর অল্প আগে ট্রান্সিটো আরিজা খাটের নিচে নানা পাত্রে লুকিয়ে রাখা তাঁর সোনাদানা, মণিমুক্তা, নানা পাথর পাড়ার ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিলিয়ে দেন, ওদের বলেন যে ওরা ইচ্ছা করলে লজেন্সের মতো এগুলি খেয়ে ফেলতে পারে। সব চাইতে মূল্যবান জিনিসগুলি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। ফ্লোরেন্টিনো আরিজা তাঁকে প্রাক্তন ‘ঈশ্বরের হাত’ খামারে কবর দেয়, ওটা তখনো ‘কলেরা গোরস্থান’ নামেই পরিচিত ছিল। ফ্লোরেন্টিনো মায়ের কবরের ওপর একটা গোলাপ চারা লাগায়।
সমাধি ক্ষেত্রে কয়েকবার যাওয়ার পর ফ্লোরেন্টিনো আরিজা একদিন আবিষ্কার করলো যে তার মায়ের খুব কাছেই সমাহিত হয়েছে অলিম্পিয়া জুলেটা। তার কবরে কোন সামাধি ফলক নেই কিন্তু সিমেন্টের বুকে আঁকি-বুকি করে তার নাম ও তারিখ লেখা হয়েছে। ফ্লোরেন্টিনোর মনে হল ব্যাপারটা লোমহর্ষক, ওর স্বামীর একটা রক্তলোলুপ কৌতুক বিশেষ। ফ্লোরেন্টিনো তার লাগানো গোলাপ গাছে গোলাপ ফোটার পর, কেউ কাছে পিঠে না থাকলে অলিম্পিয়ার কবরের ওপর একটা গোলাপ রেখে দিতো, পরে মায়ের গোলাপের ঝাড় থেকে একটা শাখা কেটে নিয়ে এসে সে ওর কবরের ওপর রোপণ করে। দুটি ঝাড়ই এক সময় এত বড় হয়ে ওঠে এবং সেখানে এত ফুল ফুটতে থাকে যে ওদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ফ্লোরেন্টিনো আরিজাকে বড় কাঁচি ও বাগান পরিচর্যার অন্যান্য হাতিয়ার নিয়ে আসতে হয়। কিন্তু কাজটা তার সাধ্যের বাইরে চলে যায়। কয়েক বছর পরে গোলাপের ঝাড়গুলি বাড়তে বাড়তে জঙ্গলের মতো হয়ে অন্যান্য কবরেও ছড়িয়ে পড়ে এবং তখন থেকে লোকজন মহামারীর নিরলঙ্কার গোরস্থানটিকে গোলাপকুঞ্জের সমাধিক্ষেত্র বলে অভিহিত করতে থাকে। কিন্তু জনৈক নগরপাল তাঁর বিশেষ প্রজ্ঞায় এক রাতে সমস্ত গোলাপ ঝাড় কেটে ফেলে গোরস্থানের প্রবেশ তোরণে একটা প্রজাতন্ত্রী ফলক বসিয়ে তার নতুন নামকরণ করলেন, ‘সর্বজনীন সমাধিক্ষেত্র।’
মায়ের মৃত্যুর পর ফ্লোরেন্টিনো আরিজা আবার ক্ষ্যাপার মতো তার কাজগুলি চালিয়ে যেতে লাগলো- অফিস, তার নিয়মিত রক্ষিতাদের কাছে হিসাব করে পালাক্রমে যাওয়া, কমার্শিয়াল ক্লাবে ডমিনো খেলা, সেই একই ভালোবাসার বই-পুঁথি পড়া আর রবিবার রবিবার সমাধিক্ষেত্র পরিদর্শন করা। এটা ছিল বাঁধাধরা জীবনের হতশ্রী মরিচা, এটাকেই সে ঘৃণা ও ভয় করতা, কিন্তু এটাই তাকে নিজের বয়স সম্পর্কে সচেতনতার হাত থেকে রক্ষা করে। কিন্তু ডিসেম্বরের এক রবিবার একটা ঘটনা ঘটলো। ইতিমধ্যে কবরের বুকে গাজিয়ে ওঠা গোলাপের ঝাড়ের কাছে তার বাগানের কাঁচি হার মেনেছিল। হঠাৎ সদ্যস্থাপিত বৈদ্যুতিক তারের ওপর কয়েকটি সোয়ালো পাখি তার চোখে পড়লো, আর তখনই আকস্মিক তার খেয়াল হল মায়ের মৃত্যুর পর কত দিন পার হয়ে গেছে, অলিম্পিয়া জুলেটা খুন হওয়ার পর কত কাল কেটে গেছে, অন্য আরেকটা সুদূর ডিসেম্বরের এক অপরাহ্নে ফারমিনা ডাজা তাকে হ্যাঁ বলেছিল, জানিয়েছিল যে সে তাকে চিরকাল ভালোবাসবে, তার পর থেকে কতো সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত তার আচার-আচরণ দেখে মনে হত যে তার ধারণায় সময় আর সবার জন্য বয়ে যাবে কিন্তু তার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে এক জায়গায়। মাত্ৰ গত সপ্তাহে হঠাৎ রাস্তায় তার এক দম্পতির সঙ্গে দেখা হয়, তার লেখা চিঠির ফলেই ওদের বিয়ে হয়েছিল, ওদের বড় ছেলে ছিল তারই ধর্মপুত্র, কিন্তু সে তাকে চিনতে পারে নি। নিজের বিব্রত অবস্থা লুকাবার জন্য সে গতানুগতিক উক্তি করলো, ‘বাপস, ও যে ইতিমধ্যে একজন পুরোদস্তুর ভদ্রলোক হয়ে গেছে!’ তার শরীর তাকে প্রথম সতর্ক সঙ্কেতগুলি পাঠাবার পরও সে আগের চালচলনই অব্যাহত রাখে, কারণ তার ছিল প্রায়শ অসুস্থ মানুষের লৌহকঠিন শারীরিক গঠন। ট্রান্সিটো আরিজা বলতেন, ‘যে একমাত্র রোগে আমার ছেলে ভুগেছে তা হল কলেরা।’ তিনি অবশ্য স্মৃতিভ্রষ্ট হবার অনেক আগেই প্রেম আর কলেরার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছিলেন। তবে তিনি ভুল করেছিলেন, তাঁর ছেলে ছয় বার ব্লেনোরহাগিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ছিল, যদিও ডাক্তারের মতে ছয় বার নয়, প্রতি বার পরাভূত হবার পর ওই একই রোগের পুনরাবির্ভাব ঘটে। তাছাড়াও তার ছিল একটা স্ফীত লিমফ গ্ল্যান্ড, চারটা আঁচিল আর কুঁচকির কাছে ছয় বার দেখা দেয়া চর্মরোগ, তবে সে বা অন্য কেউ এগুলিকে রোগ বলে মনে করতো না, এগুলি ছিল শুধু যুদ্ধের উপঢৌকন।
চল্লিশ বৎসর বয়সের সময় শরীরের বিভিন্ন জায়গায় অস্পষ্ট ব্যথা বোধ করাতে ফ্লোরেন্টিনো ডাক্তারের কাছে যায়। ডাক্তার অনেকগুলি পরীক্ষা করাবার পর বললেন, ‘বয়স।’ সে বাড়ি ফিরে আসে, তার মনে হল এসবের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নাই। নিজের অতীতের সঙ্গে তার একটাই সম্পর্ক-সূত্র ছিল, ফারমিনার সঙ্গে যা জড়িত একমাত্র তাই তার জীবনের হিসাব-নিকাশের জন্য প্রয়োজনীয়। তাই সেদিন বৈদ্যুতিক তারের ওপর সোয়ালো পাখিগুলি দেখার পর একেবারে প্রথম দিকের স্মৃতি থেকে শুরু করে সে তার সমগ্র অতীতের একটা পর্যালোচনা করলো। তার পূর্ব-পরিকল্পনাহীন প্রেম-ভালোবাসা, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার আসনে পৌঁছবার জন্য অসংখ্য চোরাগর্ত এড়ানো, অগণিত ঘটনাবলী যা তার মধ্যে ওই তিক্ত সঙ্কল্পের জন্ম দেয় যে সব কিছু সত্ত্বেও, সকল প্রতিকূলতার মুখে, ফারমিনা ডাজা তার হবে এবং সে ফারমিনা ডাজার, এই সব কিছু সে যখন পর্যালোচনা করলো তখন সে উপলব্ধি করলো যে তার জীবন পার হয়ে যাচ্ছে, আর তার নাড়ি-নক্ষত্র পর্যন্ত কেঁপে উঠলো, বার্ধক্যের প্রথম ধাক্কাতেই যেন ধরাশায়ী না হয় সেজন্য সে গোরস্থানের দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো।
‘কিন্তু কী কাণ্ড! ওসব তো ঘটেছিল ত্রিশ বছর আগে’, আতঙ্কিত হয়ে সে বলে উঠলো।
ঠিক তাই! ফারমিনা ডাজার জীবনেরও ত্রিশ বছর পার হয়ে গেছে, তবে তা ছিল তার জীবনের সব চাইতে আনন্দময় ও উদ্দীপনাপূর্ণ সময়। কাসালডুয়েরো প্রাসাদের বিভীষিকাময় দিনগুলি অতীতের আবর্জনার স্তূপে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। সে বাস করছিলো লা মাঙ্গায় তার নতুন বাড়িতে, আপন নিয়তির একচ্ছত্র কর্ত্রী, সঙ্গে তার স্বামী, তাকে যদি আবার নির্বাচন করতে বলা হত তাহলেও সে পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে তাকেই বেছে নিতো, তার ছেলে পারিবারিক ঐতিহ্য অনুসরণ করে মেডিক্যাল স্কুলে আছে, আর তার মেয়ে ওই বয়সে সে নিজে যেমন দেখতে ছিল হুবহু সে রকম, এত এক রকম যে মাঝে মাঝে তার মনে হত সেই বুঝি দ্বিতীয় বার জন্মগ্রহণ করেছে। প্রথম বারের দুর্ভাগ্যজনক ইউরোপ ভ্রমণের পর সে ঠিক করেছিল আর ওখানে যাবে না, কিন্তু সে এর পর আরো তিন বার ইউরোপ ভ্রমণ করে।
ঈশ্বর নিশ্চয়ই কোনো এক জনের প্রার্থনায় কর্ণপাত করেছিলেন। পারীতে দু’বছর কাটাবার পর, ফারমিনা ডাজা ও জুভেনাল উরবিনো যখন সবেমাত্র তাদের ভালোবাসার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যা অবশিষ্ট ছিল তা খুঁজে পেতে আরম্ভ করেছিল ঠিক তখুনি দুপুর রাতে তারা একটা টেলিগ্রাম পেলো, ডোনা ব্লাঙ্কা ডি উরবিনো মারাত্মক অসুস্থ, আর প্রায় তার পরপরই আরেকটা টেলিগ্রাম এলো তাঁর মৃত্যুসংবাদ নিয়ে। কালবিলম্ব না করে তারা প্রত্যাবর্তন করল। ফারমিনা ডাজা একটা লম্বা ঢোলা কালো পোশাক পরে জাহাজ থেকে নামলো। ওই ঢোলা পোশাকেও তার অবস্থা ঢাকা পড়ে নি। সে আবার গর্ভবতী হয়েছে। সংবাদটা একটা জনপ্রিয় গানের জন্ম দিল, যার মধ্যে বিদ্বেষপরায়ণতার চাইতে বেশি ছিল চটুল দুষ্টামি, ওই গানের ধুয়া সারা বছর ধরে শোনা যায় : ‘ও ওখানে গিয়ে কি করে বলে তোমাদের মনে হয়, আমাদের ভুবনের এই সুন্দরী? যখনই পারী থেকে ফিরে আসে তখনই দেখা যায় জন্মদান করতে সে খুবই প্রস্তুত।’ গানের কথার স্থূলতা সত্ত্বেও, ডাক্তার উরবিনো যে এসব ব্যাপার খোশ মেজাজে গ্রহণ করতে পারেন তা দেখাবার জন্য তিনি বহু বছর ধরে সোশ্যাল ক্লাবে নাচের সময় ওই গানটি গাইবার অনুরোধ জানাতেন।
মারক্যুইস ডি কসোলডুয়েরোর অস্তিত্ব বা তাঁর বংশ মর্যাদার পরিচয়বাহী নকশা বা চিত্রের কোন প্রামাণিক লিখিত দলিল পাওয়া যায় নি। কাসালডুয়েরোর মহান প্রাসাদ বেশ শোভন মূল্যে মিউনিসিপাল ট্রেজারির কাছে বিক্রি হল, তারপর যখন এক ডাচ গবেষক এখানেই ক্রিস্টোফার কলম্বসের প্রকৃত কবর অবস্থিত তা প্রমাণ করার জন্য খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করলেন, এটা ছিল এ জাতীয় পঞ্চম উদ্যোগ, তখন ওই প্রাসাদ অত্যন্ত চড়া মূল্যে আবার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বিক্রি করা হয়। ডাক্তার উরবিনোর বোনেরা কোন রকম আনুষ্ঠানিক ব্রত গ্রহণ না করে সালেসিয়ানদের মঠে নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসিনীর জীবনযাপনের জন্য চলে গেল, আর লা মাঙ্গায় নিজের নতুন বাড়ি তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হবার পূর্ব পর্যন্ত ফারমিনা ডাজা বাস করতে থাকে তার বাবার পুরনো বাড়িতে। নতুন বাড়ির কাজ সম্পূর্ণ হলে সে ওখানে প্রবেশ করলো দৃঢ় পদক্ষেপে, কর্তৃত্বভার নেয়ার জন্য প্রস্তুত, মধুচন্দ্রিমার সময় কেনা যেসব আসাবাবপত্র তারা দেশে ফেরার সময় সঙ্গে নিয়ে এসেছিলো এবং তাদের পুনর্মিলনী সফরের পর ঘর সাজাবার জন্য তারা যেসব জিনিস কিনেছিল সব সঙ্গে নিয়ে ফারমিনা তার নতুন বাড়িতে ঢুকলো, তারপর প্রথম দিন থেকেই নানা বিচিত্র পশুপাখি দিয়ে সে তার বাড়ি পূর্ণ করে ফেলতে শুরু করে। ওদের কেনার জন্য সে নিজে আন্টিল থেকে আসা পালতোলা জাহাজে গিয়ে উঠতো। সে তার নতুন করে জিতে নেয়া স্বামীসহ, যে ছেলেকে সে শোভন সুন্দর যথাযথ ভাবে গড়ে তুলেছে সেই ছেলেসহ, তাদের প্রত্যাবর্তনের চার মাস পরে যে মেয়ের জন্ম হয় এবং তারা যার নাম রাখে ওফেলিয়া সেই মেয়েসহ তার গৃহে প্রবেশ করলো। ডাক্তার উরবিনো উপলব্ধি করলেন যে মধুচন্দ্রিমার দিনগুলিতে তিনি তাঁর স্ত্রীকে যে রকম সম্পূর্ণ অধিকার করতে পেরেছিলেন তা আর সম্ভব হবে না, কারণ তাঁর আকাঙ্ক্ষিত ভালোবাসা ও শ্রেষ্ঠ সময়টা ফারমিনা এখন দান করছে তার ছেলেমেয়েদের, তবে তারপরও যা অবশিষ্ট ছিল তা নিয়েই বাঁচার ও সুখী হবার শিক্ষা তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তারা দুজন যে সুন্দর সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের গভীর প্রত্যাশী ছিলেন তা একদিন হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে তার চূড়ান্ত বিন্দুতে পৌঁছে গেল। তারা একটা বিশাল আনন্দঘন ভোজ সভায় যোগ দেন। পরিবেশিত একটি খাবার ফারমিনা ডাজার কাছে খুব সুস্বাদু বোধ হয়, খাবারটা কি তা সে বুঝতে পারলো না। প্রথমেই সেটা তার এতো ভালো লাগে যে সে দ্বিতীয়বার একই পরিমাণ আবার তার প্লেটে তুলে নেয়। সুশীল শিষ্টাচার যে তাকে তৃতীয় বার ওই খাবার নেয়ার অনুমতি দেয় না সেজন্য সে দুঃখিত হল, আর তখনই সে জানলো যে-অভাবিত আনন্দের সঙ্গে এই মাত্র যে খাবার সে খেয়েছে তা ছিল বেগুনের তরকারির একটা ঘ্যাট। ফারমিনা ভালো ভাবে তার পরাজয় মেনে নেয় এবং এর পর থেকে তাদের লা মাঙ্গার বাড়িতে বেগুনের নানা রকম রান্না নিয়মিত পরিবেশিত হতে থাকে, কাসালডুয়েরোর প্রাসাদে যে রকম হত প্রায় সেই রকমই ঘন ঘন। খাদ্য তালিকায় বেগুনের অন্তর্ভুক্তি সবাই এতো উপভোগ করে যে ডাক্তার জুভেনাল উরবিনো তাঁর বার্ধক্যের অলস মুহূর্তগুলি মাধুর্যমণ্ডিত করার জন্য প্রায়ই জের দিয়ে বলতেন যে তাঁর আরেকটি কন্যা সন্তান চাই, তা হলে এই গৃহের সব চাইতে প্রিয় শব্দ দিয়ে তিনি তার নাম রাখতে পারবেন : বেগুনি উরবিনো।
এই সময়েই ফারমিনা ডাজা বুঝতে পারে যে জনসাধারণের সামনে প্রকাশ্য জীবন এবং ব্যক্তিগত জীবন এক রকম নয়। ব্যক্তিজীবন প্রায়শ পরিবর্তনশীল, সেখানে কোন রকম ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। ছোটদের আর বড়দের মধ্যে আসল পার্থক্য কোথায় সেটা নির্ধারণ করা তার পক্ষে সহজ হয় নি। শেষ পর্যন্ত সে ছোটদেরকেই প্রাধান্য দেয়, কারণ তাদের মতামত ছিল অধিকতর নির্ভরযোগ্য। ওই সময় ফারমিনা সবেমাত্র পরিপক্বতার দিকে মোড় নিয়েছে, শেষ পর্যন্ত মোহমুক্তি ঘটেছে তার, অল্প বয়সে ইভাঞ্জেলস পার্কে সে যে রকম হবার স্বপ্ন দেখেছিল সে-রকম সে কখনোই হয় নি। তার পরিবর্তে যা হয়েছে তা নিজের কাছেও স্বীকার করার সাহস তার হত না, সে হয়েছে এক মহামূল্যবান ঝলমলে দাসী। সমাজে সে হয়ে উঠেছে সব চাইতে বেশি ভালোবাসার পাত্রী, সবাই তার জন্য কিছু করতে পারলে কৃতার্ঘ বোধ করে, সবাই তাকে ভীষণ ভয়ও করে, কিন্তু অন্য সব কাজের তুলনায় নিজের গৃহের ব্যবস্থাপনায় সে ছিল অসম্ভব কঠোর ও খুঁতখুঁতে, সেখানে কোন ত্রুটি সে ক্ষমা করতো না। সব সময় তার মনে হত যে স্বামী তাকে তার জীবনটা ধার দিয়েছেন। সুখের এক বিশাল সাম্রাজ্যের অবিমিশ্র সম্রাজ্ঞী সে, তার স্বামী সেটা নির্মাণ করেছেন এবং শুধু তার নিজেরই জন্য। সে জানতো যে সব কিছুর উপরে, এই পৃথিবীতে সবার চাইতে বেশি, তাকেই ভালোবাসেন তাঁর স্বামী কিন্তু সেটা তাঁর নিজের জন্য : সে নিয়োজিত আছে তার স্বামীর পূতপবিত্র সেবায়।
তাকে যদি কোনো কিছু বিরক্ত করতো তাহলে সেটা ছিল দৈনন্দিন খাওয়া দাওয়ার অন্তহীন পালা। শুধু যে ঠিক সময়ে খাবার পরিবেশন করতে হবে তাই নয়, পরিবেশিত খাবারকে হতে হবে নিখুঁত এবং তাঁর স্বামীকে জিজ্ঞাসা করা ছাড়াই তাঁর যা পছন্দ ঠিক তাই পরিবেশেন করতে হবে। গার্হস্থ্য জীবনের অসংখ্য অর্থহীন নিষ্প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে ফারমিনা যদি কখনো তাঁকে জিজ্ঞাসা করতো তাহলে তিনি খবরের কাগজ থেকে চোখ না তুলেই বলতেন, “দিও একটা কিছু।” তাঁর অমায়িক ভঙ্গিতে তিনি সত্যি কথাই বলতেন, সত্যিই তাঁর চাইতে কম স্বৈরাচারী কোনো স্বামীর কথা কল্পনা করা যায় না, কিন্তু খাবার সময় হলে দেখা যেতো যে একটা কিছু হলে চলতো না, তাঁর যা পছন্দ ঠিক তাই টেবিলে থাকা চাই, যেমন ভাবে চান অবিকল তেমন ভাবে। যখন অ্যাসপারাগাসের মৌসুম নয় তখনও তা পরিবেশন করতে হত, দাম যতো চড়াই হোক, যেন তিনি নিজের সুরভিত প্রস্রাবের বাষ্প থেকে আনন্দ লাভ করতে পারেন। ফারমিনা তাঁকে কোন দোষ দিত না, সে দোষ দিত জীবনকে। তবে ওই জীবনে তাঁর স্বামীই হলেন নিষ্করুণ প্রধান চরিত্র। বিন্দুমাত্র সন্দেহ হলেই তিনি তাঁর প্লেট ঠেলে দিয়ে বলতেন, “এটা তৈরি করা হয়েছে ভালোবাসা ছাড়া।” ওই অঙ্গনে তাঁর মধ্যে অবিশ্বাস্য অনুপ্রেরণার সঞ্চার হত। একবার ক্যামোমিল চায়ে এক চুমুক দিয়েই বলেন, “এর মধ্যে জানালার স্বাদ পাচ্ছি।” তাঁর স্ত্রী ও ভৃত্যকুল অবাক হয়ে যায়, কেউ সেদ্ধ করা জানালা খেয়েছে এমন কথা তারা কখনো শোনে নি, কিন্তু বিষয়টা বুঝবার জন্য তারা যখন ওই চা পান করলো তখন তারা ঠিকই বুঝলো, সত্যিই জানালার স্বাদ পাওয়া যায় তার মধ্যে। তিনি ছিলেন নিখুঁত স্বামী। তিনি মেঝে থেকে কখনো কিছু তুলতেন না, কিংবা কোন দরজা বন্ধ করতেন না। ঊষার অন্ধকার লগ্নে তাঁর জামার বোতাম নেই দেখলে ফারমিনা তাঁকে বলতে শুনতো, “একটা মানুষের দুজন স্ত্রী থাকা উচিত, একজন ভালোবাসার জন্য, অপরজন জামার বোতাম লাগাবার জন্য।” প্রতিদিন কফির পেয়ালায় প্রথম চমুক দিয়েই, স্যুপের প্রথম চামচ মুখে ঢেলেই, তিনি মর্মান্তিক চিৎকার করে উঠতেন, তাতে অবশ্য এখন আর কেউ ভয় পায় না, চিৎকারের পর তিনি বলতেন, “একদিন আমি যখন বাড়ি ছেড়ে পালাবো তখন বুঝবে যে জিভ পোড়াতে পোড়াতে অতিষ্ঠ হয়ে আমি গৃহ ত্যাগ করেছি।” তিনি আরো বলতেন, জোলাপ নেবার কারণে তিনি যেদিন খেতে পারবেন না সেদিনই বিশেষ রুচিকর ও অগাতানুগতিক খাবার তৈরি করা হয়। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর স্ত্রী বিশ্বাসঘাতকতা করে এরকম করেন। শেষে, তাঁর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীও জোলাপ না নিলে ডাক্তার জোলাপ নিতে অস্বীকৃতি জানালেন।