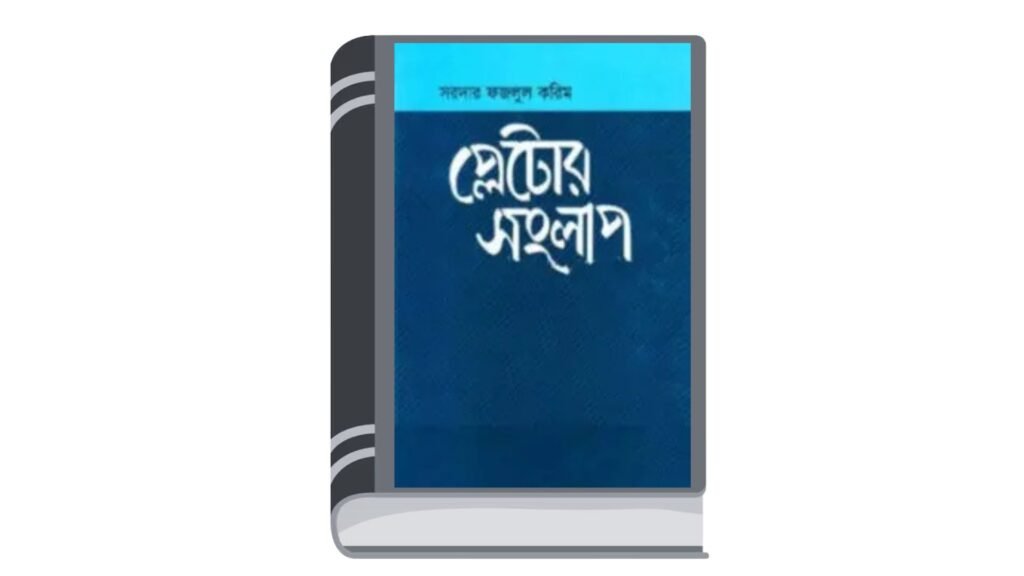চারমিডিস
চরিত্রাবলি
সক্রেটিস [কথক]
চারমিডিস
ক্রিটিয়াস
চারেফন
স্থান
আরকন প্রাসাদের অলিন্দের নিকটবর্তী তাউরিস কুস্তিমঞ্চ।
.
মাত্র গতকাল আমি সামরিক ছাউনি থেকে ফিরে এসেছি। অনেকদিন যাবৎ শহর থেকে বাইরে থাকার পরে ফিরে এসেই আমার পুরোনো আড্ডাখানাগুলোতে যাওয়ার একটা বাসনা হলো। তাই মন্দিরের অপর দিকে অবস্থিত রাজপ্রাসাদের অলিন্দের নিকটবর্তী কুস্তিশালায় গিয়ে আমি উপস্থিত হলাম। আড্ডাখানাটা তখন বেশ সরগরম। অনেক চেনামুখের সাথে নূতন মুখের উপস্থিতিও তথায় আমার নজরে পড়ল। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আমার প্রত্যাবর্তনটা ছিল আকস্মিক। তাই আমার দর্শনে বিস্মিত বন্ধুবর্গ উচ্চরবে আমাকে সংবর্ধনা জানাল। চারেফন তো প্রায় পাগল। সে ছুটে এসে আমার হাত জড়িয়ে ধরে বলল : কেমন করে তুমি ফিরে এলে সক্রেটিস (একটু ব্যাখ্যা দিয়ে বলি, সম্প্রতি পটিডিয়াতে একটা যুদ্ধ হয়ে গেছে। সে খবর আমার ফিরে আসার পূর্বেই এথেন্সে যে পৌঁছে গেছে, সেটি বুঝা যাচ্ছে।)।
চারেফনের বিস্মিত প্রশ্নের জবাবে আমি বললাম : ‘কেন এই তো আমি তোমাদের সামনেই রয়েছি?
চারেফন বলল : তা নয়। আমরা শুনেছিলাম, পটিডিয়াতে সাংঘাতিক সংঘর্ষ ঘটে গেছে, বহু লোক তাতে হতাহত হয়েছে।
সে খবর মিথ্যা নয়।
নিশ্চয়ই তুমি সেখানে ছিলে?
হ্যাঁ, ছিলাম বই কী।
তা হলে তুমি বস। বসে আমাদের যুদ্ধের সব কাহিনীটা বল। আমরা এখনো সম্পূর্ণটা শুনি নি।
আমি তখন তাদের মাঝে ক্যালেক্রাসের পুত্র ক্রিটাসের পাশে বসে পারস্পরিক অভিনন্দন বিনিময়ের পরে তাদের যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রশ্নাদির জবাব দিয়ে ঘটনাটি বিবৃত করলাম।
তাদের প্রশ্নের পালা শেষ হলে আমি শহরের খবরাদি জিজ্ঞেস করলাম। বিশেষ করে দর্শনজগতের এবং এথেন্সের যুব-সম্প্রদায়ের বর্তমান হালচাল সম্পর্কে আমার কৌতূহল নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলাম। আমি জানতে চাইলাম, সম্প্রতি-কালে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে জ্ঞান বা সৌন্দর্য, কিংবা উভয়গুণে গুণী উল্লেখযোগ্য কোনো যুবক তৈরি হয়েছে কি না?
আমার প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে ক্রিটিয়াস কুস্তিমঞ্চের প্রধান প্রবেশপথের দিকে দৃষ্টি ফেরাল। প্রবেশপথের দিকে তখন একদল জীবনোচ্ছল তরুণ উচ্চগ্রামে পরস্পরের মধ্যে আলাপ করতে করতে এগিয়ে আসছিল। পেছনে জনতার একটি দলও তাদের অনুসরণ করছিল। সেদিকে দৃষ্টি দিয়ে ক্রিটিয়াস আমাকে লক্ষ্য করে বলল; সক্রেটিস, তুমি যদি সুন্দরকে দেখতে চাও তো ওদের দিকে তাকিয়ে দেখ। ওদেরকে বলতে পারো সাক্ষাৎ-সুন্দরের অগ্রবাহিনী। আর বাহিনী যখন আসছে তার সেনাপতিও নিশ্চয়ই আর দূরে নেই। তাকেও নিশ্চয়ই তুমি এখনি দেখতে পাবে।
কে সে। কার ছেলে?
ক্রিটিয়াস বলল : তার নাম চারমিডিস। আমারই ভাই-সম্পর্কিত। আমার পিতৃব্য গ্রুকনের পুত্র। তুমিও নিশ্চয়ই তাকে দেখেছ। অবশ্য তুমি যখন চলে গিয়েছিলে তখন ও অনেক ছোট ছিল।
হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি নিশ্চয়ই ওকে দেখেছি। সেই শিশু বয়সেই ওর বৈশিষ্ট্য আমার চোখে পড়েছিল। ইতোমধ্যে ও নিশ্চয়ই পুরোদস্তুর যুবক হয়ে দাঁড়িয়েছে।
এখনই তুমি তার উন্নতি স্বচক্ষে দেখতে পাবে।
ক্রিটিয়াসের কথা শেষ না হতেই চারমিডিস এসে প্রবেশ করল।
সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্পর্কে আমার তেমন কোনো ধারণা নাই সত্যি। শুভ্র রেখা দ্বারা একটি আস্ত খড়িমাটিকে বুঝার যে ব্যাপার, আমার পক্ষেও সৌন্দর্যকে বুঝা সেই ব্যাপার। কেননা, আমার চোখে প্রায় সব তরুণই সুন্দর। তবু আমি স্বীকার না করে পারিনে যে, যুবক চারমিডিসকে যখন আমি মঞ্চে প্রবেশ করতে দেখলাম, তখন তার দেহসৌষ্ঠবে আমি বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম। সমস্ত জগৎ যেন সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে পড়েছিল। চারমিডিস যখন এসে প্রবেশ করল তখন তার চারদিকে যেন মোহ এবং বিভ্রান্তির একটা জাল সে বিস্তার করে আসছিল। তাকে অনুসরণ করে একদল মুগ্ধ প্রেমিকও অগ্রসর হয়ে আসছিল। বয়স্কদের চোখে একটি সুন্দর তরুণ যে সুন্দর বলে প্রতীয়মান হবে, তাতে অবাক হওয়ার কিছু না থাকলেও আমি দেখলাম যে, তরুণদের মধ্যেও একই উচ্ছ্বাসের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। শুধু তরুণ নয়, প্রত্যেকটি শিশু পর্যন্ত অবাক বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে ছিল, যেন চারমিডিস একটি অপূর্ব সুন্দর প্রস্তরমূর্তি।
চারফেন আমাকে লক্ষ্য করে বলল : ছেলেটি সম্পর্কে তোমার কী মনে হয়, সক্রেটিস? ছেলেটির মুখখানি কত সুন্দর, দেখেছ!
সত্যি, অপূর্ব সুন্দর।
কিন্তু কেবল মুখ নয়; নিরাবরণ দেহটিকে দেখলে তুমি দেখতে পেতে তার সর্ব অঙ্গ কী সু-সম্পূর্ণ।
আমাদের এ মতামতে পার্শ্বস্থ বন্ধুবর্গ সবাই একমত হলেন।
আমি শুধু বললাম, এমন সু-সম্পূর্ণ সুন্দরকে আমি আর কখনো দেখি নি। কেবল এই সৌন্দর্যের সাথে যদি তার একটিমাত্র গুণ থেকে থাকে।
ক্রিটিয়াস সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বলল; কী সে গুণ?
আহ! তার আত্মাও যদি মহৎ হয়। আমি বিশ্বাস করি ক্রিটিয়াস, তোমাদের বংশোত এ তরুণ সে গুণেরও নিশ্চয়ই অধিকারী।
ক্রিটিয়াস জবাবে বলল : তার বহিরঙ্গটি যেমন সুন্দর, তার অন্তরটিও তেমনি সুন্দর।
তা হলে তো আফসোসের আর কিছুই নেই। তা হলে তার আবরণহীন দেহখানির দৃশ্যের চেয়ে তার মহৎ আত্মার পরিচয়ই তো সর্বপ্রথম তার কাছ থেকে গ্রহণ করা প্রয়োজন। তার যে বয়স তাতে নিশ্চয়ই সে আমাদের সাথে আলাপ করতে ভালবাসবে।
তোমার সাথে আলাপ সে খুবই ভালবাসবে। এরই মধ্যে সে একজন দার্শনিক এবং উঁচুমানের কবি হয়ে উঠেছে। এ তার নিজের মত নয়; সবাই তার সম্বন্ধে এই মতই পোষণ করে।
জ্ঞানের এই সম্মান ও বিশিষ্টতা বহুদিন যাবৎ তোমাদের বংশের অধিগত, একথা আমি জানি ক্রিটিয়াস। জ্ঞানী সলোন থেকে উত্তরধিকারসূত্রে তুমিও তাকে পেয়েছ। কিন্তু তুমি চারমিডিসকে আমাদের নিকটে ডেকে আনছ না কেন? তার বয়স যদি অল্পও হয় তা হলেও তোমার মতো ভাই এবং অভিভাবকের সামনে বসে আমাদের সাথে আলাপ করার মধ্যে অসংগত কিছুই নেই।
নিশ্চয়ই। আমি এখনি তাকে এদিকে ডেকে পাঠাচ্ছি।
আমাকে একথা বলে ক্রিটিয়াস তার পরিচারককে ডেকে বলল : চারমিডিসকে বল, আমি তাকে এদিকে ডাকছি। এখানে একজন চিকিৎসাবিদ রয়েছেন। দুদিন পূর্বে সে তার যে-অসুখের কথা বলেছে, এই চিকিৎসক তার সেই অসুখ নিরাময় করে দেবেন। তাকে এখানে আসতে বল।
তারপর আমাকে লক্ষ্য করে ক্রিটিয়াস বলল : সম্প্রতি সে প্রত্যূষের দিকে শিরঃপীড়ার অভিযোগ করছে। এ ভালোই হলো। অপর কিছু না বলে, বরঞ্চ আমরা একথাই বলি যে, তুমি তার মাথার যন্ত্রণা আরোগ্য করে দেবে। তুমিও তাকে সেরূপই বিশ্বাস করাবার চেষ্টা কর, সক্রেটিস। কেমন?
হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাতে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু ও কি আসবে?
নিশ্চয়ই আসবে–সেজন্য ভেবো না।
ক্রিটিয়াসের আদেশ পেয়ে তরুণ চারমিডিস এসে আমার এবং ক্রিটিয়াসের। মাঝখানটিতে আসন গ্রহণ করল। আহ! তাকে আসন দেওয়ার জন্য সমবেত সবার মধ্যে সে কী উত্তেজনা এবং আগ্রহ। পরস্পর পরস্পরকে ঠেলে দিয়ে তার জন্য স্থান করতে এমন ব্যস্ত হলো যে কাউকে উঠে দাঁড়াতে হলো, কাউকে বা তার নির্দিষ্ট আসনের প্রান্ত থেকে পড়ে যেতে হলো। আমার নিজের মনোভাবের কথা বলতে গিয়ে আমাকে একথা স্বীকার করতেই হয় যে, একটা অস্বস্তিতে যেন আমার মন ভরে উঠছিল। তার সাথে আলাপের যে আত্মবিশ্বাস আমার এতক্ষণ ধরে ছিল, সে যেন লোক পেয়ে গেল। ক্রিটিয়াস যখন আমাকে দেখিয়ে বলল, আমিই সেই চিকিৎসক যার জন্য তাকে সে ডেকে পাঠিয়েছে, তখন সে অবর্ণনীয় এ দৃষ্টি তুলে আমার দিকে চাইল। সমবেত জনতার মধ্যে সেই মুহূর্তে যেন এক আলোড়নের সৃষ্টি হলো এবং সেই মুহূর্তে ক্ষণিকের জন্য তার আবরণহীন দেহের যেন একটুখানি আভাস আমি দেখতে পেলাম। সে আভাসও যেন তীব্র শিখাবিশেষ। আমার নিজেকে সংযত রাখা যেন দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াল। সেই মুহূর্তে আমি উপলব্ধি করলাম, সিডিয়াস প্রেমের প্রকৃতিকে সঠিকভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। সুন্দর তারুণ্যের প্রসঙ্গে সাবধানবাণী উচ্চারণ করে তিনি বলেছিলেন : “সিংহের সম্মুখে মৃগশাবককে তুমি এনো না” এ বাণীর যথার্থতা যেন সেই ক্ষণে আমি হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হলাম। তবু আমি নিজেকে সংযত রাখলাম এবং তার মাথার যন্ত্রণা সারাতে পারি কিনা এরূপ প্রশ্নের জবাবে কোনো প্রকারে আমি বললাম : হ্যাঁ, আমি তোমার যন্ত্রণা উপশমের ঔষধ জানি।
“কী সে ঔষধ?”–সে আমাকে পুনরায় প্রশ্ন করল।
আমি বললাম : ঔষধটি এক প্রকার বৃক্ষপত্র। কিন্তু পত্রটি প্রয়োগকালে একটি বিশেষ মন্ত্রোচ্চারণও আবশ্যক। রুগী যদি প্রত্যেক দিন ঔষধটি প্রয়োগ করে উচ্চারণ করে, তা হলে অবশ্যই সে আরোগ্য লাভ করবে। কিন্তু মন্ত্রোচ্চারণ ব্যতীত পত্র প্রয়োেগ ব্যর্থ হবে।
তা হলে আপনার মন্ত্রটি লিখে নেব।
মন্ত্রদানে আমার সম্মতি ব্যতিরেকেই, না সম্মতি নিয়ে?
স্মিতমুখে সে বলল : আপনার সম্মতি নিয়েই বটে।
বেশ বেশ! কিন্তু তুমি কি আমাকে চেনো?
আমি আপনাকে ভালো করেই চিনি। আমার সাথীদের মধ্যে আপনার সম্পর্কে কত কথা হয়। আমি যখন শিশু, তখন ভ্রাতা ক্রিটিয়াসের সাথে আপনাকে দেখতাম। তাও আমি মনে রেখেছি।
আমার জন্য এ অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, তুমি আমাকে স্মরণ রেখেছ। এবার আমি তোমাকে অনেক বেশি সহজভাবে মন্ত্র এবং নিরাময়ের ব্যাপারটি বুঝিয়ে বলতে পারব। এতক্ষণ এ সম্পর্কে আমার যে অসুবিধাবোধ ছিল, তোমার কথা শুনে এবার তা দূর হলো। কেননা আমার মন্ত্রদান শুধু তোমার শিরঃপীড়ার উপশম হবে না। তুমি নিশ্চয়ই প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদদের সম্পর্কে শুনেছ যে, কোনো রুগী যদি তাদের নিকট চোখের অসুখ নিরাময় করতে আসে তা হলে চিকিৎসকগণ বলেন, তার মাথার চিকিৎসা না করে চোখের অসুখ করা সম্ভব হবে না এবং মাথার প্রসঙ্গে বলেন যে, দেহের অন্যান্য অংশের পরীক্ষা ও চিকিৎসা ব্যতীত মাথার চিকিৎসা করা আদৌ সম্ভব নয়। যুক্তির প্রয়োগে প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদগণ রুগীর সমগ্র দেহেরই চিকিৎসা করার প্রয়াস পান। এভাবেই তারা রুগীর সম্পূর্ণ দেহ এবং তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চিকিৎসা করেন এবং যন্ত্রণাসমূহের উপশম হয়। তুমি নিশ্চয়ই এ প্রক্রিয়াকে লক্ষ করে থাকবে।
আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি এরূপ কৌশল লক্ষ করেছি।
তাদের এ প্রক্রিয়াকে যে সঠিক কৌশল, তুমি একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করবে।
নিশ্চয়ই, একথাও আমি স্বীকার করি।
তরুণের এ স্বীকৃতি আমার আলোচনায় বিশ্বাস এনে দিল। আমার নিজের প্রকাশভঙ্গিতেও অনেক স্বাভাবিকতা এল।
চারমিডিসকে উদ্দেশ করে এবার আমি বললাম : আমার মন্ত্রদানের এই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য। আমি যখন সেনাবাহিনীতে ছিলাম তখন থ্রেসরাজ জামোলজিসের এক চিকিৎসাবিদের নিকট থেকে এই জাদুমন্ত্র আমি লাভ করি। থ্রেসবাসীগণ এ বিষয়ে এত পারদর্শী যে তারা নাকি মানুষকে অমরতাও দান করতে পারে। প্ৰেসরাজ জামোলজিসের চিকিৎসাবিদদের মতে গ্রিক চিকিৎসাবিদগণের উপযুক্ত নিরাময়-প্রক্রিয়া অনেকাংশে সঠিক বটে; কিন্তু Qেসরাজ জামোলজিস বলেন যে, কোনো কোনো রুগীর চক্ষুর চিকিৎসা যদি তার মাথার চিকিৎসা ব্যতীত সম্ভব না হয়; আবার দেহের অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যতীত যদি মস্তিষ্কের চিকিৎসা না হয় তা হলে একথা ততোধিক সত্য যে, আত্মার নিরাময় ব্যতীত দেহের নিরাময় সম্ভব নয়। এখানেই গ্রিক চিকিৎসাবিদগণের অসম্পূর্ণতা এবং এজন্যই অনেক রোগের উপশম-পন্থা গ্রিকদের নিকট অজ্ঞাত। কেননা তারা সমগ্রকে বাদ দিয়ে অংশবিশেষেরই পর্যবেক্ষণ ও নিরাময় করার চেষ্টা করেন। অথচ একথা সত্য যে, সমগ্র সত্তা সুস্থ না হলে, কোনো অংশও সুস্থ থাকতে পারে না। থ্রেসরাজ জামোলজিস অবশ্যই একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি আরো বলেন : “মানুষের প্রকৃতিতে বা দেহে যা কিছু সৎ কিংবা অসৎ, ভালো কিংবা মন্দ, সব কিছুর উৎপত্তিস্থল হচ্ছে আত্মা। আত্মাতেই তার সৃষ্টি, আত্মা থেকেই তার বিস্তৃতি। এ যেন কোনো রোগের মাথা থেকে চোখের মধ্যে বিস্তার লাভ। সুতরাং দেহ বা চোখের আরোগ্যের জন্য অবশ্যই তোমাকে আত্মার আরোগ্য থেকে শুরু করতে হবে। এটাই হচ্ছে মূল কথা। মন্ত্রোচ্চারণেরও প্রয়োজন আছে। নিষ্পাপ শব্দ সমন্বয়ে তৈরি এই জাদুমন্ত্র মানুষের আত্মার সংযমের বীজ রোপণ করে। আর একথা সত্য জেনো যে, সংযম যেখানে, স্বাস্থ্যও সেখানে। সংযম শুধু কোনো বিশেষ অংশকে নয়, সমগ্র দেহকেই দ্রুত নিরাময় করে তোলে। তবে আমার মন্ত্রগুরুর একটি সতর্কবাণীও তোমাকে বলা প্রয়োজন। তিনি আমাকে সাবধান করে বলেছেন, যদি কেউ আরোগ্যের জন্য তার আত্মাকে তোমার নিকট উন্মুক্ত করে না দেয় তা হলে তুমিও যেন তার মস্তিষ্ক বা দেহের অপর কোনো অংশের চিকিৎসার জন্য মন্ত্রদান না কর। কারণ, বর্তমান যুগে চিকিৎসাবিদগণের নিরাময় প্রক্রিয়ার প্রধান দুর্বলতা হচ্ছে এই যে, তারা আত্মাকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন। এই সাথে আমার মন্ত্রমুগ্ধ আমাকে শপথ করান : ধনী কি নির্ধন, মহৎ কি সুন্দর কেউ যেন জাদুমন্ত্র ব্যতীত রোগের ঔষধ-ব্যবস্থাটি তোমার নিকট থেকে গ্রহণ করতে না পারে। সুতরাং চারমিডিস, তুমিও আমার অবস্থাটি সম্যক উপলব্ধি করতে পারবে। আমি যখন এই মর্মে। শপথ নিয়েছি, সে শপথ তখন আমাকে অবশ্যই পালন করতে হবে। এবং তোমার চিকিৎসার জন্য প্রথমে তোমার আত্মার উপরই আমার জাদুমন্ত্রের প্রয়োগ হতে হবে। তুমি যদি এতে সম্মত থাক তা হলেই ক্রমান্বয়ে আমি তোমার শিরঃপীড়াটিকেও নিরাময় করে দিতে সক্ষম হবে। অন্যথায় তোমাকে উপশম দেবার কোনো সাধ্য আমার হবে কিনা বলা শক্ত।
আমার একথা শুনে সপ্রশংসভাবে ক্রিটিয়াস বলল : শিরঃপীড়া উপলক্ষে যদি তোমার দ্বারা ওর আত্মারও উন্নতি ঘটে তা হলে একথা বলতেই হবে যে, মাথার যন্ত্রণাটি আমার স্নেহাস্পদের উপর আশীর্বাদ রূপেই এসেছে। আর একথা বলতে আমার দ্বিধা নেই, চারমিডিস তার সমবয়স্ক তরুণদের মধ্যে শুধু সৌন্দর্যেই শ্রেষ্ঠ নয়, অধিকন্তু যাকে তুমি জাদুমন্ত্রের ফল বলে আখ্যায়িত করেছ, সেই সংযমের গুণেও সে গুণী।
তাই নাকি? সে তো বড় আনন্দের কথা
আমি জোর দিয়েই বলতে পারি যে, মানুষের মধ্যে সংযমে সে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ এবং অপরাপর কোনো গুণেই সে তার বয়স্ক কারু চেয়ে হীন নয়।
একথা শুনে চারমিডিসকে লক্ষ্য করে আমি বললাম : এর চেয়ে বড় প্রশংসা তো আর কিছু হতে পারে না, বৎস। আমি বিশ্বাস করি, এ প্রশংসা অপাত্রে দত্ত নয়। সমস্ত গুণেই তোমার চরম উৎকর্ষ লাভ করা আবশ্যক। তোমাদের বংশের ন্যায় এমন সর্বগুণে গুণান্বিত অপর কোনো বংশের উল্লেখ কি কেউ করতে পারে? তোমার পিতৃকুলে রয়েছেন ড্রপিডাসের পুত্র ক্রিটিয়াস যার সৌন্দর্য এবং সাধুতা আনাক্রিন, সলোন এবং অন্যান্য কবি ও মনীষীদের উৎসর্গবাণীর বিষয় রয়েছে; সমধিক বিশিষ্ট তোমার মাতৃকুলে। রয়েছেন তোমার জননীর ভ্রাতা পাইরিল্যাম্পিস। পাইরিল্যাম্পিসের নাম সুনামে, সুখ্যাতিতে অনন্য। পারস্যরাজের দরবারে কিংবা এশিয়া মহাদেশের অপর যে-কোনো দেশে তিনি রাষ্ট্রদূত হিসাবে প্রেরিত হয়েছিলেন। কোথাও তাঁর সমকক্ষ অপর একজন মহৎ ব্যক্তি দৃষ্ট হয় নি। এই দুই মহৎ বংশের মিলনফল তুমি বৎস! এই অপূর্ব গুণসমূহের বংশগত উত্তরাধিকার তুমি। মহৎ গুণাবলির চরমোকর্ষ তুমি অর্জন করবে, এই তো স্বাভাবিক। গ্লকপুত্র চারমিডিস, তোমার ত্রুটিহীন অঙ্গসৌষ্ঠব তোমার পূর্বপুরুষদের সম্মানকেই বর্ধিত করে দেবে। তাই আমি বলছি, বৎস! তোমার সৌন্দর্যের সাথে যদি তুমি সংযমের যোগ সাধন করতে পার এবং তোমার ভ্রাতা ক্রিটিয়াসের প্রশংসানুযায়ী অপরাপর মহৎ গুণেও যদি তুমি ইতোমধ্যে সমৃদ্ধ হয়ে থাক, তা হলে আমি উচ্চকণ্ঠেই বলব, তুমি উপযুক্ত জননীর উপযুক্ত সন্তান বটে।
আমার বক্তব্যের প্রধান কথাও এখানে। ক্রিটিয়াস বলেছেন, তুমি সংযমের গুণেও গুণান্বিত। তোমার চরিত্রে সত্যই যদি সংযমের সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং তুমি যদি পরিপূর্ণরূপে সংযমী হয়ে থাক তা হলে জামোলজিস বা অপর কোনো মন্ত্রদাতার মন্ত্রেরই প্রয়োজন তোমার হবে না। তা হলে জাদুমন্ত্রের যেকথা আমি বলেছি সে মন্ত্র ব্যতিরেকেই তোমার শিরঃপীড়ার নিরাময়-ঔষধটি আমি প্রয়োগ করতে পারব। অন্যথায় ঔষধ। প্রয়োগের পূর্বে অবশ্যই আমাকে মন্ত্রদানের কাজটিও করতে হবে। সুতরাং এবার তুমি নিজ মুখে আমাকে বল, ক্রিটিয়াস যেমন বলেছেন তেমনিভাবে তুমি সংযমের গুণ আয়ত্ত করতে পেরেছে কিনা?
আমার এই প্রশ্নে চারমিডিসের মুখমণ্ডল লজ্জায় রক্তিম হয়ে তাকে অধিকতর সুন্দর করে তুলল। লজ্জাজড়িত কণ্ঠে সুন্দর বিনয়ের সঙ্গে তখন সে বলল : আপনার প্রশ্নের সরাসরি “হ্যাঁ কিংবা না’-রূপ জবাব দান আমার পক্ষে কষ্টকর। কেননা, যদি আমি বলি যে, আমি সংযমী নই, তা হলে আমার মুখে সেটি বিস্ময়কর শুনাবে। উপরন্তু তেমন উক্তিতে ক্রিটিয়াস এবং অপরাপর সবাই আমার সম্পর্কে যা মনে করেন তা মিথ্যা হয়ে যাবে। অপরদিকে আমি যদি বলি, হ্যাঁ, আমি সংযমী তা হলে আমার নিজমুখে সে জবাব আত্মপ্রশংসারূপ বলে প্রতীয়মান হবে। সেরূপ উত্তর হবে আমার পক্ষে অবিনয়ী ব্যবহার। কাজেই আপনার প্রশ্নটির জবাব আমার জন্য একটি উভয়-সঙ্কট স্বরূপ।
তার জবাব শুনে আমি বললাম; বৎস! তোমার এ কথাটি খুবই স্বাভাবিক ও সুন্দর। সুতরাং সরাসরি জবাব দানের চেয়ে এস তুমি এবং আমি একসাথে অনুসন্ধান করে দেখি, তোমার চরিত্রে সংযমের গুণটি সৃষ্ট হয়েছে কিনা। তা হলে আর তোমাকে অবাঞ্ছিত কোনো উত্তর দিতে হবে না এবং আমার নিরাময় প্রক্রিয়ায়ও কোনো হঠকারিতা বা ভ্রান্তির অবকাশ থাকবে না। তুমি যদি সম্মত হও, তা হলে এস আমরা উভয়ে মিলে সমস্যাটির সমাধানের চেষ্টা করি।
চারমিডিস বলল : এর চেয়ে বাঞ্ছনীয় আর কিছু হতে পারে না। আপনি যেরূপ উত্তম বোধ করেন, অনুরূপভাবেই এ বিষয়ে অগ্রসর হউন।
উত্তম বৎস! তা হলে আমি তোমাকে একটি প্রশ্ন করেই আমাদের অনুসন্ধান শুরু করব। সংযম সম্পর্কেই আমি একটি প্রশ্ন করতে চাই। কেননা, তোমার চরিত্রে যদি সংযমের সৃষ্টি হয়ে থাকে তা হলে তার কোনো-না-কোনো পরিচয় অবশ্যই তোমার জানা আছে। সেই পরিচয়টি জানতে পেলে সংযম সম্পর্কে আমাদের ধারণা গঠনে সাহায্য হবে, তাই নয় কি?
আমারও তাই মনে হয়।
তোমার মাতৃভাষাকে তুমি উত্তমরূপেই জানো। তাই তোমার মাতৃভাষাতেই এ বিষয়টি ভালো করে প্রকাশ করতে পারবে। তাই নয় কি?
আজ্ঞে।
তোমার মধ্যে সংযম আছে কি নেই, এটি বুঝবার জন্য তা হলে আমি প্রশ্ন করছি : সংযম কাকে বলে?
আমার প্রশ্ন শুনে তরুণ চারমিডিস জবাব দিতে প্রথম ইতস্তত করল। তারপর বলল; আমার মনে হয় সংযম মানে হাঁটা, চলা, বাক্যালাপ বা অনুরূপ যে-কোনো কাজকে সুশৃঙ্খল ও শান্তভাবে সম্পন্ন করা। এক কথায় বললে, সংযমের অর্থ হবে শান্তি।
অতি উত্তম, চারমিডিস। আমাদের দেখতে হবে সংযমের এই সংজ্ঞাটি কতখানি যথার্থ। একথা সত্য যে অনেকেই মনে করে যে শান্ত স্বভাব বা শান্তিই সংযম। কিন্তু একথাগুলির সঠিক অর্থ কী? আচ্ছা অপর একটি প্রশ্নও উত্থাপন কর যাক : সংযম কি মহৎ এবং মঙ্গলকর গুণসূচক নয়?
অবশ্যই।
বেশ! এবার একটি কাজের কথা ধরা যাক। যেমন লিখন-অভ্যাস। এ ব্যাপারে কোনটি উত্তম : দ্রুততার সাথে লিখন ক্ষমতা, না ধীরভাবে লিখন শক্তি?
দ্রুতভাবেই নিশ্চয়।
পঠনের প্রশ্নে? দ্রুততার সহিত, না ধীরতার সহিত? কোনটি শ্রেয়?
এ ব্যাপারেও দ্রুততার সহিত নিশ্চয়।
বক্সিং বা অনুরূপ ক্রীড়ানুষ্ঠানে?
একই কথা সত্য।
তা হলে দেখা যাচ্ছে অপরাপর কাজেও, যেমন দৌড়, লাফ প্রভৃতি শারীরিক ক্রীড়ায় দ্রুততা এবং তৎপরতাই কাম্য, ধীরতা, নিষ্ক্রিয়তা বা শান্তি সবই অবাঞ্ছিত এবং খারাপ।
তাই তো প্রমাণিত হচ্ছে।
তা হলে বলতে হয় যে, কোনো শারীরিক কার্যে শান্তি ও ধীরতার চেয়ে বরঞ্চ তৎপরতা এবং দ্রুততাই মহৎ এবং উত্তম।
আজ্ঞে, নিঃসন্দেহে।
তা হলে সংযমের বেলা? সংযম কি কাম্য?
অবশ্যই।
তা হলে শরীরের ক্ষেত্রে সেই সংযমকেই আমরা বাঞ্ছনীয় বলব, যে সংযম শরীরে ধীরতার চেয়ে তৎপরতার সৃষ্টি করে।
একথা ঠিক।
কোনো কিছু শেখার ক্ষেত্রেও কোনটিকে আমরা কাম্য বলব? দক্ষতা, না কাঠিন্যকে?
অবশ্যই দক্ষতাকে।
ঠিক কথা। শিক্ষায় দক্ষতা বলতে আমরা বুঝি দ্রুততার সাথে শেখা এবং শিক্ষায় কাঠিন্য বলতে বুঝব, যে-শিক্ষা মন্থর গতিতে কষ্টকরভাবে অগ্রসর হয়, তাকে।
আজ্ঞে।
তা হলে কাউকে শিক্ষা দেবার বেলাতেও ধীর এবং মন্থরভাবে শেখাবার চেয়ে কি দ্রুততার সাথে শিক্ষাদান শ্রেয় নয়?
দ্রুততার সাথে শিক্ষাদানই শ্রেয়।
তেমনি স্মৃতিশক্তির ক্ষেত্রেও কোনটি শ্ৰেয়? দ্রুততার সাথে স্মরণ করার ক্ষমতা, না ধীরতা ও মন্থরতার সহিত স্মরণ করার শক্তি?
অবশ্যই দ্রুততার সহিত স্মরণ করার শক্তি।
মন বা আত্মার দিকে থেকেও তৎপরতা এবং নিপুণতাকে, না মন্থরতাকে আমরা গুণ বলে মনে করি?
অবশ্যই তৎপরতা ও নিপুণতাকে।
অনুরূপভাবে লিখন বিদ্যায় কিংবা সংগীতচর্চায় বা অপর কোনো গুণাৰ্জনে দ্রুততা, না ধীরতাকে আমরা উত্তম বলে বিবেচনা করি?
সর্বত্রই দ্রুততাকে।
তেমনি আত্মার অনুসন্ধান বা পর্যবেক্ষণের বিষয়তেও আমরা কাকে প্রশংসার যোগ্য বিবেচনা করি? যে পর্যবেক্ষণে ধীর এবং অনুসন্ধানে ইতস্তত তাকে কিংবা যে স্বাচ্ছন্দ্য
ও দ্রুততার সঙ্গে অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণে সক্ষম তাকে?
অবশ্যই স্বচ্ছন্দ ও দ্রুত যার পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান-ক্ষমতা, তাকে।
কাজে কাজেই দেহ বা মন সম্পর্কিত সব বিষয়তেই কাম্য হচ্ছে সক্রিয়তা এবং তৎপরতা। তাই নয় কি?
নিঃসন্দেহে।
সুতরাং এই বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, সংযমকে আমরা ধীরতা বলতে পারিনে, কিংবা সংযমী জীবনকেও ধীর বা শান্ত জীবন বলে আখ্যায়িত করতে পারিনে। কারণ, সংযমকে আমরা কাম্য বলে বিবেচনা করেছি এবং সংযমী জীবনকে মহৎ বলেছি। কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ধীর ও শ্লথ পদ্ধতি হয় আদৌ কোনো সফলতা আনতে পারে না, অথবা খুব অল্প ক্ষেত্রেই তা সফলতা আনয়ন করে। বরঞ্চ দ্রুততা এবং উদ্যোগের সাথে কৃতকর্মের সফলতা অনেক বেশি। আর দ্বিধাহীনভাবে এতখানি না বললেও একথা অস্বীকার করা চলে না যে, ধীরতা এমন কোনো গুণ নয় যে, কেবল সেজন্যই কোনো কাজ মহৎ বলে পরিগণিত হতে পারে। ধীরতাকে গুণ হিসাবে গ্রহণ করেও বলা চলে, ধীর কাজের যত মহত্ত্ব, দ্রুত কাজের মহত্ত্ব তার চেয়ে কম নয়। কাজেই এদিক দিয়েও সংযমকে কেবল ধীরতার প্রকাশ বলা চলে। অধীর জীবনের চেয়ে ধীর জীবনের বেশি সংযমী হওয়ার কোনো নিশ্চয়তা নেই। চলা, বলা এবং অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে দ্রুততার মূল্য আমরা বিচার করেছি। তাতে দেখেছি, সংযম যেমন মহৎ ও কাম্য গুণ, তৎপরতাও তার চেয়ে কম মহৎ বা কাম্য নয় এবং ধীর যদি সংযমী হতে পারে, তৎপর ব্যক্তির পক্ষেও তার চেয়ে কোনো অংশে কম সংযমী হওয়ার কোনো কারণ নেই।
চারমিডিস বলল : আজ্ঞে আপনি যা বলেছেন তাকে সঠিক বলেই মনে হচ্ছে।
তদুপরি বৎস, এবার তুমি অন্তর্জগতের প্রতি দৃষ্টি ফেরাও। মনঃসমীক্ষা দ্বারা তুমি অবহিত হও, সংযম তোমার আত্মার উপর কি পরিফল সৃষ্টি করে এবং এই পরিফল ভোগকারী সত্তার সঠিক চরিত্র সম্পর্কে জ্ঞানী হও। এইসব সমস্যা নিয়ে চিন্তা করে দ্বিধাহীনভাবে এবার বল : সংযম কী?
আমার এ আদেশ পেয়ে তরুণ চারমিডিস কিয়ৎক্ষণ যাবৎ নিঃশব্দ হয়ে রইল। আমি বুঝলাম, তরুণ ঐকান্তিকতার সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করছে। পরিশেষে সে জবাব দিল : প্রাজ্ঞ, আমার মত হচ্ছে, সংযম মানুষকে সলজ্জ বা বিনয়ী করে তোলে এবং বিনয় ও সংযমকে আমি একই বলে বিবেচনা করি।
ধন্যবাদ বৎস! আচ্ছা একটি কথা আমি স্মরণ করিয়ে দিই। তুমি কি কিয়ৎক্ষণ পূর্বেই স্বীকার করো নি যে, সংযম মহৎও বটে?
আজ্ঞে, অবশ্যই।
এবং সংযমী যারা তারা উত্তমও বটে?
অবশ্যই।
বেশ! কিন্তু যা মানুষের মঙ্গল সাধন করে না সে গুণ উত্তম বা মঙ্গলকর বলে বিবেচিত হতে পারে?
অবশ্যই না।
কিন্তু তোমার সিদ্ধান্ত হচ্ছে, সংযম শুধু মহৎই নয়, মঙ্গলকরও বটে?
আজ্ঞে, আমি তাই মনে করি।
কিন্তু তুমি কি হোমারের এই উক্তিটি স্বীকার করবে; “বিপন্নের নিকট বিনয় মূল্যহীন?”
উক্তিটি আমি স্বীকার করি।
তা হলে অবস্থাটা দাঁড়ায় এই যে, বিনয় উত্তমও বটে, উত্তম নয়ও বটে?
স্পষ্টতই তাই।
তেমনি সংযম যখন মানুষের মঙ্গলই সাধন করে তখন সংযম অবশ্যই উত্তম। সংযমকে অবাঞ্ছিত বা খারাপ বলা যায় না।
আপনার বিশ্লেষণ থেকে তাই তো বোধ হচ্ছে।
তা হলে এ থেকে সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, বিনয় যখন উত্তমও হতে পারে, অধমও হতে পারে এবং সংযম যখন উত্তম বই অধম হতে পারে না, তখন নিশ্চয়ই বিনয় ও সংযম সহগামী হতে পারে না। অর্থাৎ সংযম বিনয় বলে বিবেচিত হতে পারে না।
জ্ঞানী, আপনি যা বলেছেন, তা সঠিক বলেই বোধ হচ্ছে। কিন্তু সংযমের’ অপর একটি সংজ্ঞা সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে আমার বিশেষ আগ্রহ হচ্ছে। কোনো জ্ঞানীর কাছ থেকে সংযমের আমি এরূপ সংজ্ঞা শুনেছি, সংযম হচ্ছে আপন কার্য সাধন।’ এরূপ সংজ্ঞা কি যথার্থ?
ওহ! দুষ্ট ছেলে! এ নিশ্চয়ই ক্রিটিয়াসের কথা বা অপর কোনো দার্শনিকের বক্তব্য।
ক্রিটিয়াস বলে উঠল : আমি নই, সক্রেটিস। এ নিশ্চয়ই অপর কারো মন্তব্য।
চারমিডিস তার প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার উপর জোর দিয়ে বলল : সংজ্ঞা কে দিয়েছে, এ প্রসঙ্গে তা কি অবান্তর নয়?
তুমি ঠিকই বলেছ বৎস! কে বলেছে সেটি গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। আমাদের জিজ্ঞাস্য হচ্ছে সংজ্ঞাটি যথার্থ কিনা।
আজ্ঞে, এ প্রশ্নে সে দৃষ্টিভঙ্গিই তো সঠিক।
নিঃসন্দেহে। তবু এ সংজ্ঞা সত্য কি মিথ্যা তা নির্ধারণ করা হয়তো আমাদের পক্ষে কখনো সম্ভব হবে না। কেননা, সংজ্ঞাটি একটি ধাঁধা স্বরূপ।
আপনি একথা কেন বলছেন?
কারণ, যিনি সংযমের এই সংজ্ঞা উচ্চারণ করেছেন, আমার মনে হয় তিনি এই সংজ্ঞা দ্বারা যা বুঝাতে চেয়েছেন তা প্রকাশ করেন নি। অর্থাৎ তিনি ভেবেছেন এক এবং বলেছেন আর। আচ্ছা, একজন লিপিকার যখন লেখে কিংবা পাঠ করে তখন সে কোনো কর্মে রত থাকে, কি থাকে না?
নিশ্চয়ই সে একটি কাজে রত থাকে।
বেশ। কিন্তু লিপিকার যখন কিছু লেখে বা পাঠ করে বা তোমাদের মতো কিশোর ও তরুণদের নামের লিখন ও পঠন শিক্ষা দেয় তখন কি তোমরা শত্রু-মিত্র উভয়রূপ নাম লেখ এবং পড়, কিংবা কেবল এক পক্ষীয়?
না, উভয়রূপ নামই আমরা লিখি বা পাঠ করি।
এ বিষয়ে কি তোমাদের কোনোরূপ জবরদস্তি বা হস্তক্ষেপের কথা মনে হয়েছে?
না, নিশ্চয়ই নয়।
কিন্তু লিখন ও পঠন যদি একই কাজ হয় তা হলে তোমরা লিপিকারের নির্দেশে এমন কাজও করছিলে যা তোমাদের করার আবশ্যক ছিল না।
প্রাজ্ঞ, আমি ঠিক অনুধাবন করতে পারছিনে। লিখন ও পঠন তো কাজেরই শামিল।
ঠিক ঠিক। কিন্তু নিরাময়-কৌশল, নির্মাণ-কলা, বয়নশিল্প কিংবা যা-কিছু নিষ্পন্ন করতেই শিল্পকলার আবশ্যক হয় তাদের সবই কি কাজ নয়?
অবশ্যই।
তাই যদি হয়, তা হলে তুমি কি মনে কর যে, একটি রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় যদি এরূপ বিধান বিধিবদ্ধ হয় যে, প্রত্যেক নাগরিক তার আপন বস্ত্রকে বয়ন করবে, আপন পরিধেয়কে ধৌত করবে, আপন পাদুকাকে প্রস্তুত করবে, অনুরূপভাবে আপন প্রয়োজনের প্রত্যেকটি বস্তুকেই সে নিজে তৈরি করবে, অপরের প্রয়োজনীয় কোনো কাজ সে করবে না, তা হলে সে রাষ্ট্রের পরিচালন কার্য সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হবে?
না, আমি তা মনে করিনে।
কিন্তু আমি মনে করি, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও যদি সংযমের প্রশ্ন থাকে তা হলে সংযমী রাষ্ট্র অবশ্যই একটি সুশৃঙ্খল রাষ্ট্র।
অবশ্যই।
তা হলে বলা চলে না যে, “সংযম হচ্ছে আপন কার্য সাধন”। অন্তত উপরে আমরা যেভাবে উল্লেখ করেছি, সেভাবে সংযম দ্বারা কেবল ‘নিজ কার্য সাধন’ বুঝানো চলে না।
স্পষ্টতই তা সম্ভব নয়। এইমাত্র আমি তাই বলেছিলাম যে, যিনি সংযমকে ‘আপন কার্য সাধন’ বলে আখ্যায়িত করেছেন, তিনি নিশ্চয়ই অপর কোনো অর্থকে বুঝাতে চেয়েছেন। কেননা তিনি তো মূর্খ নন যে সংযমকে তিনি এইরূপে ব্যাখ্যা করবেন। তোমাকে যিনি এই সংজ্ঞা বলেছেন তাকে তুমি নিশ্চয়ই মূর্খ বলবে না, কি বল চারমিডিস?
আজ্ঞে। বরঞ্চ আমি তাকে একজন বিশেষ জ্ঞানী লোক বলেই বিবেচনা করি।
তা হলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, তিনি এই সংজ্ঞাকে একটি ধাঁধা হিসাবেই তৈরি করেছেন। তিনি মনে করেন যে, নিজ কার্য সাধন’ সংজ্ঞার সঠিক অর্থ কেউ অনুধাবন করতে সক্ষম হবে না।
এবার আমারও তাই বোধ হচ্ছে।
আচ্ছা, এবার দেখা যাক, ‘নিজ কার্য সাধন’ কথাটির সঠিক অর্থ কি হতে পারে? চারমিডিস, তুমি কি বলতে পার ‘নিজ কার্য সাধন’ বলতে কি বুঝায়?
আজ্ঞে না, এ কথার সঠিক অর্থ আমি এখন বুঝতে পারছিনে। বিস্ময়ের কিছু হবে না যদি সংজ্ঞাকার নিজেই এই কথাটির অর্থ আদৌ কিছু না বুঝে থাকেন।
একথা বলে হেসে উঠে চারমিডিস দুষ্টামির বাকা চাহনিতে ক্রিটিয়াসের দিকে দৃষ্টি ফেরাল।
আমিও ক্রিটিয়াসের দিকে তাকালাম। বহুক্ষণ যাবই ক্রিটিয়াসের মধ্যে একটি অস্থিরতার ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল। এতক্ষণ অবধি সে নিজেকে সংযম রেখেছিল। কিন্তু এখন যেন তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ল। এবার আমার পূর্বের সন্দেহে স্থির নিশ্চিত হলাম যে, সংযমের এই সংজ্ঞার সাথে ক্রিটিয়াসের অবশ্যই কোনো সম্পর্ক রয়েছে। চারমিডিস নিশ্চয়ই সংযমের এই সংজ্ঞা ক্রিটিয়াসের নিকট থেকেই পেয়েছে। দুষ্ট চারমিডিস এ যাবৎ আমার প্রশ্নসমূহের জবাব নিজে না দিয়ে ক্রিটিয়াস দ্বারা দেওয়াবার প্রয়াস পাচ্ছিল। এজন্য তাকে সে উত্তেজিত করে তুলছিল। চারমিডিস এমন ভাব প্রকাশ করছিল যেন সংযমের এই সংজ্ঞা আমাদের আলোচনায় আর যথার্থ বলে প্রমাণিত হচ্ছে না। বরঞ্চ আমাদের বিশ্লেষণে এই সংজ্ঞার খণ্ডন ঘটেছে। এ অবস্থা দেখে ক্রিটিয়াস যেন ক্রমান্বয়ে রেগে যাচ্ছিল। কোনো কবি আবৃত্তিকারীর সঙ্গে ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হয়, ক্রিটিয়াসও যেন চারমিডিসের সঙ্গে একটা ঝগড়ায় রত হতে যাচ্ছিল। ক্রিটিয়াস এবার কঠিন দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বলল : চারমিডিস, তুমি নিজে বুঝতে অক্ষম বলেই কি মনে করছ যে সংযমের এই সংজ্ঞাকার আপন শব্দ কয়টির অর্থ বুঝতেও সক্ষম নয়?
আমি বললাম : বন্ধুবর ক্রিটিয়াস, রাগ কর না। চারমিডিসের যে তরুণ বয়স তাতে তার কাছ থেকে এই সংজ্ঞার অর্থ উপলব্ধি খুব আশা করা যায় না। তুমি বয়সে অনেক বড়, তোমার জ্ঞান অনেক বেশি। তাই তোমার কাছ থেকেই স্বাভাবিকভাবে সংযমের এই সংজ্ঞাটির ব্যাখ্যা আশা করা যেতে পারে। কাজেই সংযম সম্পর্কে চারমিডিস যে সংজ্ঞা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করেছে সে সংজ্ঞাকে যদি তুমি গ্রহণ কর, তার শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা নিয়ে চারমিডিসের সহিত তর্ক করার চেয়ে আমি তোমার সহিত আলোচনা করাই শ্রেয় মনে করি।
সক্রেটিস, তোমার বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত এবং আমি একথাও বলছি যে, সংযমের এই সংজ্ঞাকে আমি স্বীকার করি।
অতি উত্তম, বন্ধু! তা হলে আমার প্রশ্নটা আবার উপস্থিত করতে দাও : আমি এইমাত্র বলছিলাম, প্রত্যেক শিল্পী বা কারিগরই কোনো-না-কোনো কাজ করে। তুমি কি একথা স্বীকার কর?
হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।
বেশ। তারা কি শুধু নিজেদের কাজই সম্পন্ন করে, না অপরের কার্য সম্পন্ন করে?
তারা অপরের জন্যও দ্রব্যাদি তৈরি করে বা কাজ করে।
কিন্তু তারা যখন কেবল নিজ কার্যই সাধন করে না, অপরের কাজও যখন করে, তখন কি তাদের সংযমী বলা চলে?
কেন নয়?
না, না, তাদের সংযমী বলতে আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু যিনি সংযমকে নিজ কার্য সাধন’ বলেন এবং তৎপরই বলেন, অপরের কার্য সাধনকারীকেও কেন সংযমী বলা চলবে না, তার জন্য কি কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি হয় না?
না, সক্রেটিস, তা নয়। আমি কি কখনো বলেছি, অপরের কাজ’ যে করে সেও সংযমী? আমি বলেছি, অপরের জন্য যারা কিছু প্রস্তুত করে।
ক্রিটিয়াস! কী বলছ তুমি? তুমি কি তা হলে বলতে চাও যে কাজ করা এবং প্রস্তুত করা এক কথা নয়?
না। বরঞ্চ কাজ করা এবং প্রস্তুত করাকে তুমি যতখানি এক মনে কর, আমি এ দুটিকে তার চেয়ে বেশি পৃথক মনে করিনে। আমি এ শিক্ষা হিসিয়ডের নিকট থেকেই পেয়েছি। হিসিয়ড বলেছেন, “কাজে কোনো লজ্জা নাই।” একথা ঠিক। কিন্তু কাজ বলতে তিনি নিশ্চয়ই তোমার বর্ণিত কার্যাবলি, যেমন পাদুকা প্রস্তুত, কাসুন্দি বিক্রয় বা দেহ বিক্রয় প্রভৃতিকে বুঝান নি। তা হলে আর তিনি কাজে কোনো লজ্জা নেই কথাটি বলতে পারতেন না। সুতরাং সক্রেটিস, কাজ বলতে এ সমস্ত কাজকে আমরা বুঝাতে পারিনে। আমার ধারণা হিসিয়ড কাজ করা এবং প্রস্তুত করার মধ্যে একটি পার্থক্য স্বীকার করেছেন। তিনি যেমন বলেছেন, কাজে কোনো লজ্জা নেই’ তেমনি অসম্মানজনক বা হীন কাজ যে লজ্জার বিষয় তাও তিনি বলেছেন। তাই তিনি মহৎ কাজকেই কাজ’ বলেছেন। আবার যা ক্ষতিকর তাকে মানুষের উপযুক্ত কাজ বলে অভিহিত করেন নি। এবং তাই অর্থেই হিসিয়ড বা অপর যে-কোনো জ্ঞানী ব্যক্তিই ‘আপন কার্য সাধনকারীকে’ জ্ঞানী বলে আখ্যায়িত করতে পারেন।
ক্রিটিয়াস, তুমি মুখ খুলতেই বুঝতে পারছিলাম যে, মানুষের জন্য যা বাঞ্ছনীয় এবং নিজস্ব তাকে তুমি মঙ্গলকর বলেই অভিহিত করবে–এবং মঙ্গলকর কাজকেই মাত্র তুমি কাজ বলবে। শব্দ বা নামের মধ্যে এই সমস্ত পার্থক্যের সাথে প্রডিকাস প্রভৃতির রচনার মারফত আমি কম পরিচিত নই। কাজেই ক্রিটিয়াস, তুমি যে-কোনো শব্দে যে কোনো অর্থ আরোপ করতে পার, তাতে আমি আপত্তি করব না। কিন্তু আমার আবেদন, বক্তব্যে তুমি আর একটু সহজ এবং বোধগম্য হয়ো। আমার প্রশ্ন : কার্য সম্পাদন করা অথবা কোনো দ্রব্য প্রস্তুত করা’–অর্থাৎ যে-কোনো শব্দ দ্বারাই এ সবকে তুমি আখ্যায়িত কর না কেন, মানুষের মঙ্গলকর এ সমস্ত কাজকে কি তুমি সংযম বলে অভিহিত করতে চাও?
হ্যাঁ সক্রেটিস, আমি তাই বলব।
তা হলে, যে-কেবল মঙ্গলই সাধন করে, সে-ই সংযমী। উপরন্তু যে অমঙ্গল সাধন করে সে সংযমী হতে পারে না?
হ্যাঁ, তাই। আর এ তো কেবল আমারই মত নয়, তুমিও নিশ্চয় একথাই বলবে।
আমি যাই বলি না কেন, আমাদের আলোচ্য তা নয়। তুমি যা বলেছ, আমরা বর্তমানে তাই নিয়ে আলোচনা করছি।
ক্রিটিয়াস এবার নিজেকে ব্যাখ্যা করে বলল : আমার বক্তব্য হচ্ছে, যে-ব্যক্তি অমঙ্গল সাধন করে, কোনো মঙ্গল সাধন করে না, সে ব্যক্তি সংযমী হতে পারে না; অপরদিকে যে মঙ্গল সাধন করে এবং অমঙ্গল সাধন করে না সে ব্যক্তিই সংযমী। সহজ কথায় বলব : সংযম হচ্ছে মঙ্গলকর বা সঙ্কর্মের সাধন।
ক্রিটিয়াস, ধরা যাক তোমার বক্তব্য ঠিক। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, তুমি কি মনে কর, সংযমী ব্যক্তি আপন সংযম সম্পর্কে অজ্ঞ বা অচেতন হতে পারে?
না, তা আমি মনে করিনে।
কিন্তু তুমি কি খানিকক্ষণ পূর্বেই বল নি যে, একজন কারিগর আপন কাজের সাথে অপরের কাজও নিষ্পন্ন করতে পারে?
হ্যাঁ, তা আমি বলেছি; কিন্তু তোমার অভিপ্রায় কী সক্রেটিস?
আমার কোনো অভিপ্রায় নেই ক্রিটিয়াস। তুমি শুধু আমাকে বল, যে চিকিৎসক রোগীকে নিরাময় করে তোলেন তিনি কি একই সাথে নিজের এবং অপরের মঙ্গল সাধন করতে পারেন?
তিনি তা পারেন বলেই আমার বোধ হয়।
এবং যিনি তা করেন তিনি কর্তব্যও নিষ্পন্ন করেন?
হ্যাঁ।
বেশ। এবং যে নিজ কর্তব্য সম্পাদন করে সে কি একই সাথে সংযম ও জ্ঞানের সাথেই কাজ করে না?
হ্যাঁ, অবশ্যই সে সংযম ও জ্ঞানের সাথে কাজ করে।
কিন্তু একজন কি সর্বদা জানতে পারে কখন তার চিকিৎসা প্রণালী রোগীর পক্ষে উপকারী হবে এবং কখন হবে না? অথবা কারিগরের কথাই ধরা যাক। সে কি নিঃসন্দেহে বুঝতে পারে কোন কাজ তার উপকার সাধন করে এবং কোন কাজ উপকার করে না?
তা সর্বদা সে জানতে পারে না।
তা হলে সে কোনো কোনো সময়ে নিজের অজ্ঞাতেও আপন কার্য দ্বারা মঙ্গল বা অমঙ্গল উভয়ই সাধন করতে পারে। অথচ মঙ্গল সাধনের মনোভাবের জন্য তার সম্পর্কে বলা হবে যে, জ্ঞান কিংবা সংযমের সাথেই আপন কার্য করে চলেছে। তুমি তো একথাই বলেছ?
তা বলেছি।
তা হলে বিষয়টি এরূপ দাঁড়ায় যে, ব্যক্তি আপন জ্ঞান বা সংযম সম্পর্কে অজ্ঞ থেকেও মঙ্গল সাধনের ব্যাপারে জ্ঞান বা সংযমের সাথেই আপন কার্য সম্পাদন করতে পারে।
কিন্তু সক্রেটিস, এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের অযোগ্য। তোমার বিশ্লেষণে আমার কোনো বক্তব্য বা স্বীকৃতির ফল হিসাবে যদি এরূপ সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয় যে, ‘অজ্ঞানীও সংযম এবং জ্ঞানের কর্তব্য সম্পাদনে সক্ষম, তা হলে বরঞ্চ এরূপ সিদ্ধান্ত স্বীকারের চেয়ে আমি আমার পূর্বোক্ত অভিমতকেই প্রত্যাহার করে নিব। এ-বিষয়ে আমার ভ্রান্তি স্বীকারে কোনো সঙ্কোচ আমি বোধ করব না। কেননা, আমি মনে করি যে, আত্মজ্ঞানই হচ্ছে জ্ঞানের মূল ভিত্তি। এবং তাই ভবিষ্যদ্বাণীর স্থল ডেলফীতে উৎকর্ণ ব্যক্তি, তুমি আপনাকে জানো’ বাণীটির যথার্থতা আমি স্বীকার করি। এ বাণীর তাৎপর্য এই যে, প্রবেশকারীকে লক্ষ্য করে যেন দেবতা বলছেন, “সাধারণ এই যে, কেমন আছ প্রভৃতি অভিবাদনসূচক শব্দ বাঞ্ছনীয় নয়। তার চেয়ে ভালো হচ্ছে, মানুষ যদি পরস্পরকে উদ্দেশ করে বলে, তুমি সংযমী হও বা আপনি সংযমী হউন। উপরের বাণীটির উৎকীর্ণদাতার উপলব্ধি নিশ্চয়ই এই ছিল যে, দেবতা যখন উপাসনাকারীর নিকট নিজেকে প্রকাশ করে, তখন সাধারণ ভাষাতে আত্মপ্রকাশ করে না। প্রকাশিত ভাষার একটা গূঢ়ার্থও থাকে; এবং তাই ভক্তের দল মন্দিরে প্রবেশ করে এই বাণীই শুনতে পায়; “ভক্তবৃন্দ! তোমরা সংযমী হও।” কিন্তু এই কথাটিও ঐশ্বরিক বাণীর রহস্যময়তা নিয়ে উচ্চারিত হয়। কেননা নিজেকে জানো’ এবং সংযমী হয়ে কথা দুইটির অর্থ একই। তথাপি আক্ষরিকভাবে তারা ভিন্ন এবং এজন্যই তাৎপর্য উপলব্ধিতেও ভ্রান্তি এসেছে। এই ভ্রান্তির জন্যই পরবর্তী ঋষিগণ এই বাণীর সাথে যোগ করে বলেছেন : “অত্যধিকতার আশ্রয় নিও না; প্রতিশ্রুতি দানে পাপ নিকটবর্তী হয়।” এ সবই অর্থকে ভ্রান্তভাবে উপলব্ধি করার ফল। কারণ, এই ঋষিগণ মনে করেছেন যে মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণবাণী আপনাকে জানো’ দেবতার উপদেশামৃত, ভক্তের প্রতি প্রবেশকালে দেবতার অভিবাদন নয়। এই মনোভাব থেকে তারাও উপদেশাবলিকে বৃদ্ধি করে গিয়েছেন।
আমার এ সমস্ত কথা বলার উদ্দেশ্য কী? সক্রেটিস, এ সমস্ত কথার উত্থাপন এজন্য যে, পূর্বের আলোচনার চেয়ে, এস, আমরা বরঞ্চ কোনো নূতন বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করি। পুরোনো আলোচনা থেকে এতক্ষণ অবধি আমরা কোনো ফল লাভ করেছি বলে মনে হয় না। হতে পারে তুমি অথবা আমি যুক্তিতে শুদ্ধ। কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট ফল যে আমরা আমাদের আলোচনায় লাভ করতে পারি নি, সেকথা ঠিক। নূতন আলোচনায় আমি প্রমাণ করতে প্রয়াস পাব যে : “সংযম হচ্ছে আত্মজ্ঞান।”
ক্রিটিয়াস, তোমার প্রস্তাবের আমি বিরোধিতা করিনে। কিন্তু তোমার একটি মনোভাবে আমার আপত্তি রয়েছে। তুমি এমনভাবে তোমার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছ যেন, তোমাকে যে প্রশ্ন আমি জিজ্ঞাসা করেছি সে প্রশ্নের জবাব আমি জানি এবং কেবল ইচ্ছা করলেই প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারতাম। কিন্তু এ অনুমান যথার্থ নয়, ক্রিটিয়াস। প্রশ্নের জবাবে আমি আদৌ জানিনে। আমি অনুসন্ধান করে দেখতে চাই কোনটি সত্য, কোনটি সত্য নয়। সে সন্ধান আমি যখন লাভ করবো, তখন নিশ্চয়ই তোমাকে বলব, তোমার সাথে আমি একমত কিংবা একমত নই। কাজেই এ প্রসঙ্গেও আমাকে চিন্তা করতে দাও।
নিশ্চয়ই। তুমি চিন্তা কর।
আমি চিন্তা করে দেখেছি, তোমার উত্থাপিত নূতন সংজ্ঞার ক্ষেত্রেও অবস্থাটি হচ্ছে এই যে, সংযম যদি জ্ঞান হয়, তা হলে অবশ্যই তাকে বিজ্ঞান হতে হবে এবং যদি সে বিজ্ঞান হয় তা হলে সে বিজ্ঞানের বিশেষ বিষয়বস্তুও থাকতে হবে।
হ্যাঁ, সংযম হচ্ছে জ্ঞান এবং জ্ঞানকে যদি বিজ্ঞান বল তো সে জ্ঞানেরই বিজ্ঞান।
বেশ! তুমি জানো, চিকিৎসাশাস্ত্রও একটি বিজ্ঞান; কিন্তু তার বিষয়বস্তু হচ্ছে স্বাস্থ্য, তাই নয় কি?
হ্যাঁ, তাই।
এখন তুমি যদি আমাকে জিজ্ঞাসা কর যে, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বা ভেষজশাস্ত্রের ফলাফল বা উপকারিতা কী, তা হলে আমি বলব, স্বাস্থ্যরক্ষা বা গঠনে ভেষজশাস্ত্রের বিরাট অবদান রয়েছে।
ভালো কথা।
তুমি যদি প্রশ্ন কর, স্থাপত্যবিদ্যা অর্থাৎ নির্মাণকৌশলের যে বিজ্ঞান তার অবদান কী তা হলে আমি গৃহাদির উল্লেখ করব। সমস্ত বিদ্যা বা বিজ্ঞান সম্পর্কেই এই কথা সত্য। তাদের প্রত্যেকেরই ভিন্ন বিষয় এবং উপকারিতা রয়েছে। ক্রিটিয়াস, অনুরূপভাবে তোমাকে এবার সংযম বা জ্ঞান সম্পর্কেও প্রশ্নটি করা যাক। তুমি সংযমকে জ্ঞান এবং জ্ঞানকে জ্ঞানেরই বিজ্ঞান বলেছ। তা হলে তুমি বল, অপরাপর বিজ্ঞানের ন্যায় এই বিজ্ঞানের ফল উপকারিতা কী?
সক্রেটিস, তোমার এই অনুসন্ধান পদ্ধতি আমি সঠিক বলে মনে করিনে। কেননা, জ্ঞানকে তুমি অপরাপর বিজ্ঞানের মতো একটি সাধারণ বিজ্ঞান বলে ভাবতে পার না। অথচ তোমার প্রশ্ন এবং আলোচনা থেকে বোধ হচ্ছে, তুমি জ্ঞানকে যে-কোনো বিজ্ঞানের অনুরূপ বিজ্ঞান বলে ধরে নিচ্ছ। কিন্তু একটি বিজ্ঞান যেমন অপর থেকে পৃথক, জ্ঞানও তেমনি অপরাপর বিজ্ঞান থেকে পৃথক। এই সমস্ত বিজ্ঞানের মধ্যেও গণন বিজ্ঞান বা জ্যামিতির কথা ধর। গৃহাদি যেরূপ নির্মাণ-বিজ্ঞানের ফল, পোশাক যেমন বয়নবিজ্ঞানের ফল, তেমনিভাবে গণনবিজ্ঞানের বিষয় হিসাবে তুমি কোনো বস্তুর উল্লেখ করতে পার? নিশ্চয়ই তুমি এস্থলে কোনো বস্তুর কথা উল্লেখ করতে সমর্থ হবে না।
তা ঠিকই বলেছ। তবু এ সমস্ত বিজ্ঞানের একটি করে বিষয় আছে যাকে বিজ্ঞান থেকে আলাদা করা সম্ভব। বিজ্ঞানের বিষয়’ কথাটি বলতেই পার্থক্যটি লক্ষ করা যায়। গণনবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও দেখানো চলে যে, গণনবিজ্ঞানের বিষয় হচ্ছে জোড়-বেজোড় সংখ্যার পারস্পরিক সংখ্যাগত সম্পর্ক নির্ধারণ। একি ঠিক নয়?
হ্যাঁ তা ঠিক।
কিন্তু জোড়-বেজোড় সংখ্যাগুলোই গণনবিজ্ঞান নয়?
তা নয়।
ধর, ওজনবিজ্ঞান। ওজনকৌশলেরও বিষয় হচ্ছে হাল্কা-ভারী বস্তুর ওজন নির্ধারণ। কিন্তু ওজনকৌশল এবং হালকা-ভারী বস্তু দুটি কথা এক নয়, এ তো তুমি স্বীকার করবে?
হ্যাঁ।
তা হলে এবার তুমি বল, জ্ঞানের এমনকি বিষয় আছে যা ‘জ্ঞান’ নয়–কিন্তু যা নিয়েই তৈরি হয়েছে ‘জ্ঞানের বিজ্ঞান’?
সক্রেটিস, তুমি পুনর্বার একই ভুল করছ বলে আমি মনে করি। তুমি প্রথমে প্রশ্ন করেছ, সংযম ও জ্ঞানের সাথে অপরাপর বিজ্ঞানের পার্থক্য কী? কিন্তু তার পরেই তুমি সাধারণ বিজ্ঞানের সাথে জ্ঞানের অভিন্নতা বার করার প্রয়াস পাচ্ছ। কিন্তু তুমি জান যে, এই দুয়ের মধ্যে ঐক্য নেই। কেননা সাধারণ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটা করে ভিন্ন বিষয়বস্তু থাকে। কোনো বিজ্ঞানের বিষয়ই বিজ্ঞান নয়, একটি নির্দিষ্ট কোনো বিদ্যা বা কৌশলচর্চাই তার বিষয় : উপরন্তু জ্ঞানই একমাত্র বিজ্ঞান যে হচ্ছে বিজ্ঞানেরই বিজ্ঞান এবং আপন সত্তা–অর্থাৎ জ্ঞানেরই বিজ্ঞান, ভিন্নতর কোনো বিষয়ের নয়। তুমি এ সম্পর্কে সম্যকরূপেই অবগত আছ। তথাপি তুমি পূর্বে যা অস্বীকার করেছ, বর্তমানকে পুনরায় সেই পন্থাই অবলম্বন কর। তুমি আলোচনাটি স্বাভাবিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবার বদলে আমাকে খণ্ডন করারই চেষ্টা করছ।
কিন্তু ক্রিটিয়াস তোমাকে যদি খণ্ডন করতে চাই, তাতে আমার অপরাধ কোথায়? তোমাকে খণ্ডন করার উদ্দেশ্য আমার জ্ঞানকেই পরীক্ষা করা বই অন্য কিছু তো নয়। যা আমি জানিনে তাকে জানি বলে দাবি করার অহমিকা অচেতনভাবেও যেন আমি প্রকাশ না করি, সেই জন্যই আমার এই প্রশ্ন উত্থাপন। সত্যিকারভাবে বলতে গেলে, বিষয়টির বর্তমান আলোচনা আমি নিজের স্বার্থে এবং বলতে পার কিয়ৎপরিমাণ আমার সুহৃদবর্গেরও স্বার্থে চালাচ্ছি। কেননা, সত্যের সন্ধান তো কোনো ব্যক্তি বিশেষের জন্য নয়, সমগ্র মানবজাতির জন্যই কল্যাণকর।
ক্রিটিয়াস বলল : নিশ্চয়ই সক্রেটিস।
তা হলে প্রিয় বন্ধু, যে প্রশ্ন আমি করেছি তার ওপর তোমার মতামত তুমি ব্যক্ত কর-সক্রেটিস খণ্ডিত হলো, কিংবা ক্রিটিয়াস খণ্ডিত হলো, তা নিয়ে মনঃকষ্ট পেয়ো না। যুক্তির গতির প্রতি লক্ষ দাও এবং প্রমাণফল কী দাঁড়ায় সেটি বিবেচনা কর।
সক্রেটিস, তোমার এ বক্তব্য আমি সঠিক বলেই মনে করি। আমি এখন থেকে তোমার আদেশ অনুযায়ী যুক্তিকেই অনুসরণ করব।
তা হলে তুমি আমায় দয়া করে বল, জ্ঞান দ্বারা তুমি কী বুঝাতে চাও?
আমি বুঝাতে চাই যে, জ্ঞানই একমাত্র বিজ্ঞান যে হচ্ছে অপর সব বিজ্ঞানের বিজ্ঞান এবং সত্তা, অর্থাৎ জ্ঞানেরই বিজ্ঞান।
কিন্তু তুমি যখন ‘জ্ঞানকে’ বিজ্ঞানের বিজ্ঞান বলে অভিহিত কর তখন একথাটিও এসে পড়ে যে, ‘জ্ঞান অ-বিজ্ঞানেরও বিজ্ঞান’–তাই নয় কি?
অবশ্যই।
তা হলে বিষয়টি দাঁড়ায় এইরূপ : জ্ঞানী বা সংযমী ব্যক্তিই মাত্র নিজেকে জানে–অর্থাৎ কি সে নিজে জানে এবং জানে না, উভয়কেই সে জানে, তদুপরি, অপর সবাই কী জানে না, তথাপি মনে করে যে তারা তা জানে–এসব কিছুই একমাত্র জ্ঞানী বা সংযমী ব্যক্তিই জানতে পারে, অপর কেউ নয়। এবং একেই তুমি বলতে চাচ্ছ সংযম, জ্ঞান এবং আত্মজ্ঞান। অর্থাৎ ব্যক্তির পক্ষে যা সে জানে, তাই জানা এবং যা সে জানে না তাকেও জানা। ক্রিটিয়াস তোমার কথার এই তো গূঢ়ার্থ?
হ্যাঁ, তাই।
তা হলে জিউসের নাম করে সর্বশেষ যুক্তিটি নিয়ে এস। এবার আমরা আলোচনা আরম্ভ করি। এবার আমাদের মূল প্রশ্নটিই হচ্ছে : কোনো ব্যক্তির পক্ষে কি আদৌ সম্ভব যে নিজে যা জানে এবং জানে না–উভয়কেই সে জানে? এবং আদৌ যদি এটি সম্ভব হয়–অর্থাৎ বিশেষ করে, এরূপ যদি ভাবা যায়, তা হলেও এই জ্ঞানের সার্থকতাই বা কি?
হ্যাঁ, নিশ্চয়ই এই প্রশ্নটিই আমাদের বিবেচ্য।
এখানেই আমি তোমার সাহায্যপ্রার্থী, ক্রিটিয়াস। যুক্তির এই জালেই আমি আটকে গেছি। আমার সত্যকার অসুবিধার কথাটি তোমায় বলতে চাই।
হ্যাঁ বল। আমি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করব।
জ্ঞান সম্পর্কে তুমি যেকথা বলছ তাই যদি সত্য হয় তা হলে পরিস্থিতিটি এরূপ দাঁড়ায় না যে : এমন একটি বিজ্ঞান আছে যে বিজ্ঞানের বিজ্ঞান এবং অ-বিজ্ঞানেরও বিজ্ঞান এবং যে নিজেই নিজের বিষয়বস্তু?
ঠিক।
প্রিয় বন্ধু, কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখ, কী অসংগত এই পরিস্থিতি। অনুরূপ অপর যে-কোনো দৃষ্টান্তে পরিস্থিতির অবিশ্বাস্যতা তোমার নিকট স্বচ্ছ হয়ে ধরা পড়বে।
তা কী করে হয়? অনুরূপ অপর কি দৃষ্টান্তের কথাই বা তুমি বলছ, সক্রেটিস?
ধর দৃষ্টিশক্তির কথা। মনে কর এক ব্যক্তির এমন এক বিশেষ রকমের দৃষ্টিশক্তি বা চক্ষু রয়েছে যে নিজেকে দেখে, অপরের দৃষ্টিশক্তিকে দেখে এবং অপরের দৃষ্টিশক্তির অভাবকেও দেখে। তুমি কি এরূপ কোনো দৃষ্টিশক্তির চিন্তা করতে সক্ষম?
না, তা কী করে সম্ভব?
অথবা ধর শ্রবণশক্তি। এমন শ্রবণেন্দ্রিয়কে কি তুমি কল্পনা করতে পার যে নিজের শব্দ, অপরকে শব্দ ও শব্দহীনতা ব্যতীত অপর কিছু শ্রবণ করতে পারে না?
না, এমন কেনো শ্রবণেন্দ্রিয়ও নেই।
মানুষের অপর সব ইন্দ্রিয়কেই ধর। এমন কোনো ইন্দ্রিয়ের কথা কি চিন্তা করা চলে
যে নিজেকে এবং অপরের জানে, কিন্তু চেতনার কোনো বিশেষ বস্তুকে জানে না?
না এরূপ চিন্তা করা চলে না।
আচ্ছা, ভেবে দেখ, এমন কোনো কামনা কি থাকা সম্ভব যে শুধু কামনারই কামনা, কিন্তু বিশেষ কোনো সুখ, আনন্দ বা কাম্য বস্তুর কামনা নয়?
না, অবশ্যই নয়।
কিংবা ইচ্ছা? এমন আকাঙ্ক্ষা কি হতে পারে যার আকাঙ্ক্ষার প্রতি আকাক্ষা ব্যতীত অপর বিশেষ কিছুর প্রতিই আকাঙ্ক্ষা নেই?
না, এরূপও চিন্তা করা চলে না।
অথবা ধর প্রেম বা ভালবাসার কথা। এমন কোনো ভালবাসার কথা কি ভাবা চলে যে অবয়বহীন ভালবাসা ব্যতীত কোনো সুন্দরকে বা ভালবাসার অপর কোনো বস্তুকে ভালবাসে না?
না, এরূপও ভাবা চলে না।
কিংবা ধরা যাক ভীতি। এমন কোনো ভয় আছে যে নিজেকে অর্থাৎ ভয়কেই ভয় করে, কিন্তু ভয়ের কোনো বস্তুকে ভয় করে না?
না, এমন কোনো ভয়কে আমি জানি না।
শেষত ধরা যাক ‘মত’ কথাটিকে। এমন কোনো অভিমত কি আছে যে শুধু অভিমতেরই অভিমত, কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের অভিমত নয়?
অথচ আমরা কিন্তু এমন এক বিজ্ঞানের কথা বলছি, যে বিজ্ঞানের বিজ্ঞান ব্যতীত অপর কোনো নির্দিষ্ট আলোচ্য বিষয়ই নেই।*
[* ‘জ্ঞান নিজেকে জানে’ ‘দৃষ্টিশক্তি নিজেকে দেখে’ ইন্দ্রিয় নিজেকে বোধ করে প্রভৃতি বাক্য ইংরেজির ‘Wisdom known itself Vision viewing itself Sense sensing itself’ কথাগুলির অনুবাদ হলেও বাংলা অনুবাদ ইংরেজির মূল অর্থকে অনেক সময়ে যথাযথ জোর এবং স্পষ্টতা দিয়ে প্রকাশ করতে পারে। ব্যাখ্যা ব্যতীত অনুবাদের সীমাবদ্ধতায় প্রকাশের কিয়ৎ-পরিমাণ অস্পষ্টতা অনিবার্য।–অনুবাদক]
হ্যাঁ আমাদের কথাটি তাই দাঁড়িয়েছে।
কিন্তু সত্য কথাটি কী অদ্ভুত। এরূপ কোনো বিজ্ঞান আদৌ সম্ভব নয়, এমন সিদ্ধান্ত এখনও আমরা গ্রহণ করছিনে। বিষয়টি নিয়ে আর একটু আলোচনা করা যাক।
তুমি ঠিকই বলেছ, সক্রেটিস।
যে বিজ্ঞান সম্পর্কে আমরা আলোচনা করছি, একথা তো অনস্বীকার্য যে, সে বিজ্ঞানের অবশ্যই কোনো বিষয়বস্তু থাকতে হবে। কেননা, অর্থগতভাবও কোনো বিশেষ কিছুর জ্ঞান বলেই তো বিজ্ঞান।
একথা ঠিক।
যেমন, কোনো কিছুকে যদি বৃহত্তর বলা হয় তা হলে স্বাভাবিকভাবেই বুঝতে হবে যে, অপর কোনো বিশেষ কিছুর তুলনায় বস্তুটি বৃহৎ।
হ্যাঁ, অবশ্যই।
এবং তুলিত বস্তুটি অপরটির চেয়ে ক্ষুদ্র।
নিশ্চয়ই।
এবার এমন কোনো বস্তুকে যদি পাওয়া যায় যে বস্তু নিজের থেকে এবং অপর অনেক বৃহৎ বস্তু থেকেও বৃহৎ; কিন্তু এই অনেক বস্তু যে বস্তুর চেয়ে ক্ষুদ্র তার চেয়ে আমাদের কল্পিত বস্তুটি বৃহৎ নয়, তা হলে এই বস্তুটি একই সাথে নিজের চেয়ে বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র বলে বিবেচিত হবে।
এটাই তো অপরিহার্য অনুমান বলে বোধ হয়।
আবার, কোনো ‘দ্বিগুণ’ যদি নিজের তুলনায় এবং অপরাপর দ্বিগুণের তুলনায় দ্বিগুণ হয়, তা হলে এই সমস্ত দ্বিগুণ, কল্পিত দ্বিগুণের অর্ধেক বলে বিবেচিত হবে। কেননা, ‘দ্বিগুণ’ এবং ‘অর্ধেক’ কথা দুটি পরস্পর আপেক্ষিক।
একথা ঠিক।
অর্থাৎ যাকে তার নিজের চেয়েও বৃহৎ কিংবা গুরু কিংবা প্রবৃদ্ধ বলব, সে একই কালে ক্ষুদ্রতর, লঘুতর বা তরুণতর বলেও বিবেচিত হবে। অন্য কথায় কোনো ভাব বা কথাকে তার নিজের সত্তার সাথে তুলনা করে উল্লেখ করলে তার মধ্যে তার অন্তর্ভুক্ত বস্তুর স্বভাবেরও প্রতিফলন ঘটবে। তাই নয় কি?*
[* অধ্যাপক জোয়েটের ইংরেজি অনুবাদেও স্থানটি হেঁয়ালিপূর্ণ বলে বোধ হয়। দার্শনিক শব্দ ও ভাবের সহজবোধ্য প্রকাশ অনেকক্ষেত্রে দূরূহ। ভাষান্তরের বেলা এই অসুবিধা প্রকটতর হয়ে দেখা দেয়। সক্রেটিসের বক্তব্যও তাই এ স্থলে জটিল ও দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। সংলাপের” নায়কের বক্তব্য সম্ভবত এই যে, বস্তুহীন ভাব অকল্পনীয়। আর অবশ্যই কোনো বস্তু বা বিষয়ের ভাব। এবং সেই বস্তু বা বিষয়ের চরিত্র নিরপেক্ষ ভাবের কোনো অস্তিত্ব বা প্রকৃতি চিন্তা করা চলে না।–অনুবাদক]
অবশ্যই।
কাজেই তুমি যদি বল, শ্রবণ নিজেকে অর্থাৎ শ্রবণ শ্রবণকে শ্রবণ করে, তা হলেও বলতে হবে যে শ্রবণ একটা শব্দকে শুনছে : শব্দ বাদে অপর কিছু বা শব্দহীনতা বা শূন্যতার শ্রবণ সম্ভব নয়।
স্বীকার্য।
তোমার দৃষ্টি সম্পর্কে যদি আমরা বলি যে, দৃষ্টি নিজেকে অর্থাৎ দৃষ্ট ব্যতীত অপর কিছু দেখে না, তা হলেও কথাটা অর্থহীন হবে। একথার অর্থ হবে, দৃষ্টি অবশ্য কোনো রংকে দেখে; কেননা চক্ষু কখনো রংশূন্য কোনো দৃশ্য বা অপর কোনো বস্তুকেই দেখতে পারে না।
না, তা পারে না।
তুমি কি একটি বিষয়ে লক্ষ করেছ ক্রিটিয়াস? যে দৃষ্টান্তগুলি আমরা উল্লেখ করেছি তাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে ‘নিজেদের সাথেই মাত্র সম্পর্ক’-বাচক ভাবটি [notion of a relation to self] আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন, আয়তন বা সংখ্যা : কোনো আয়তন বা সংখ্যা অপর কোনো বস্তুর সঙ্গে নয়, কেবল আপন ‘আয়তনত্ব’ বা ‘সংখ্যাত্বের’ সঙ্গেই সম্পর্কিত একথা বলা চলে না। আবার অপরক্ষেত্রে কথটি বিশ্বাসেরও অযোগ্য।
অবশ্যই।
যেমন শ্রবণ বা দৃষ্টি অথবা স্বয়ংক্রিয়তা বা উত্তাপের দহনশক্তি : এ সমস্ত ক্ষেত্রে অনেকে নিজের সাথে সম্পর্কসূচক ভাবটিকে বিশ্বাসের অযোগ্য ভাবতে পারে; আবার অনেকে এ সমস্ত চিন্তাকে বিশ্বাসের যোগ্যও ভাবতে পারে। আমরা বিষয়টির চূড়ান্ত মীমাংসা করতে পারিনে। এ সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে নিজের সীমাবদ্ধতাকে আমি স্বীকার করি। আমাদের প্রয়োজন শক্তিমান কোনো দার্শনিকের যিনি নিশ্চিতরূপে বলতে পারবেন, আদৌ এমন কিছু আছে কিনা যার নিজের সঙ্গে এবং অপর বস্তু নিরপেক্ষ সম্পর্ক থাকা সম্ভব; কিংবা কোন ক্ষেত্রে সম্ভব এবং কোন ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। আমি নিশ্চিত করে বলতে সক্ষম নই যে, বিষয়নিরপেক্ষ এবং আত্মনিবদ্ধ এরূপ বিজ্ঞান আদৌ হতে পারে কিনা। এমনকি, রূপ বিজ্ঞান যদি হতেও পারে, তা হলেও সে বিজ্ঞান যে ‘জ্ঞানের বিজ্ঞান’ বা সংযম, একথাও আমি ততক্ষণ অবধি স্বীকার করতে পারিনে যতক্ষণ না প্রমাণিত হয় যে, সংযম মঙ্গলকর এবং বাঞ্ছনীয়। কাজেই ক্রিটিয়াস, তুমি যখন বলেছ, সংযম বা জ্ঞান হচ্ছে ‘বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞানের বিজ্ঞান?’ তখন তুমিই আমাকে দুটি কথা বুঝিয়ে দাও; প্রথম, এরূপ বিজ্ঞানের সম্ভাব্যতা কোথায়? দ্বিতীয়, যদি বা সম্ভব, তা হলেও এর অবদান বা উপকারিতাই বা কী? এ প্রশ্ন দুটির জবাব পেলেই সংযম সম্পর্কে তোমার অভিমতটি সঠিক বলে আমি অনুধাবন করতে সক্ষম হবো।
এই বক্তব্য শ্রবণ করে ক্রিটিয়াস আমার সঙ্কটের কথা বুঝতে পারল। আমি তার পানে সমাধানের জন্য তাকালাম। কিন্তু ঘুম জড়ানো চোখে হাই তোলাটা যেমন সংক্রামক হয়ে এক থেকে অন্যে ছড়িয়ে পড়ে, আমাদের এই সঙ্কটের ক্ষেত্রেও আমার সঙ্কট ক্রিটিয়াসকেও আচ্ছন্ন করল। কিন্তু ক্রিটিয়াসের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অপরের সম্মুখে আপন দুর্বলতার স্বীকার না করে শক্তির পরিচয় দেবার চেষ্টা করা। সমস্যা সমাধানের যে দাবি আমি তার কাছে করেছি তাকে গ্রহণ করার অক্ষমতাকে বন্ধুবর্গের সম্মুখে স্বীকার করতে সে লজ্জাবোধ করছিল; ফলে তার মুখের উপর অপ্রতিভের যে চিহ্ন প্রকাশ পাচ্ছিল তাকে সে কাটাবার ব্যর্থ চেষ্টা করল। এই পরিস্থিতি থেকে তাকে উদ্ধার করার জন্য এবং আলোচনাটি যাতে অগ্রসর হতে পারে, সেজন্য আমি নিজেই বললাম : বেশ, ক্রিটিয়াস, ধরা যাক, এরূপ ‘বিজ্ঞানের বিজ্ঞান যথার্থই আছে। এই অনুমান ঠিক কিংবা ঠিক নয় সে বিচার পুনরায় পরে করা যাবে। কিন্তু এর অস্তিত্ব ধরে নিলেও প্রশ্ন থাকে : এরূপ বিজ্ঞান মারফত আমরা কি প্রকারে যা জানি এবং জানিনে অথবা আত্মজ্ঞান ও পরজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে সক্ষম হই?
তোমার কথা আমি ঠিকই মনে করি সক্রেটিস। আমিও মনে করি, আত্মজ্ঞানের যে বিজ্ঞান সে মানুষকে পরজ্ঞানেও জ্ঞানী করে তোলে। যে দ্রুতগামী সে যেমন দ্রুত চলে, যার সৌন্দর্য আছে সে যেমন সুন্দর, তেমনিভাবে যার জ্ঞান আছে সে জ্ঞানী–অর্থাৎ সে জানে এবং তার জানার ক্ষমতা আছে। আবার এই আত্মজ্ঞানের যে বিজ্ঞান সে ‘আত্মার জ্ঞানেও মানুষকে সমৃদ্ধ করে তুলবে।
এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, যার আত্মজ্ঞান রয়েছে সে আত্মার জ্ঞানে জ্ঞানী। কিন্তু তথাপি প্রশ্ন হচ্ছে, এমনকি নিশ্চয়তা আছে যে, যার আত্মজ্ঞান আছে সে অবশ্যই ‘জানা’ এবং ‘অজানা’ উভয়কেই জানতে পারবে?
ক্রিটিয়াস জবাব দিল : কারণ এরা একই বিষয়কে বুঝাচ্ছে।
আমি বললাম; হতে পারে, অসম্ভব নয়। কিন্তু আমি যে অন্ধকারে ছিলাম, এখানে সেই অন্ধকারেই রয়েছি। কেননা, আমি এখনও বুঝতে অক্ষম যে, কোনো ব্যক্তির জানা এবং অজানার জ্ঞান দ্বারা কী করে আত্মার জ্ঞান বুঝান চলে?
তুমি কী বলতে চাচ্ছ, সক্রেটিস?
আমার বক্তব্য হচ্ছে : স্বীকার করলাম আমি যে, বিজ্ঞানের বিজ্ঞান বলে কিছু রয়েছে। তা হলেও দুটি বস্তুর মধ্যে একটি বিজ্ঞান এবং অপরটি বিজ্ঞান নয়,–এই জ্ঞানটি ব্যতীত অপর কোনো জ্ঞানই কি আমরা এই বিজ্ঞানের বিজ্ঞান দ্বারা লাভ করতে পারি?
না, তা পারিনে।
আর একটি প্রশ্ন : স্বাস্থ্যের জ্ঞান বা অ-জ্ঞান এবং ন্যায়পরতার জ্ঞান ও অ-জ্ঞান কি এক?
অবশ্যই নয়।
একটি হচ্ছে ভেষজ সম্বন্ধীয়, অপরটি রাজনীতি। অথচ আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে বিশুদ্ধ জ্ঞান।
খুবই সত্য কথা।
কাজেই কেউ যদি শুধু জানে–অর্থাৎ তার কেবল ‘জ্ঞানের জ্ঞান’ থাকে, কিন্তু দেহ, ন্যায়পরতা বা অপর নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের জ্ঞান না থাকে তা হলে তার জ্ঞান অনির্দিষ্ট কিছু জানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। নির্দিষ্ট কোনো কার্যকর জ্ঞানলাভ তার ঘটবে না।
তাই দেখছি।
তা হলে ব্যক্তি যা জানে সে জানার ব্যাপারে এই ‘জ্ঞানের বিজ্ঞানের’ অবদান কী? ধর স্বাস্থ্য বিষয়ে কারো জ্ঞান আছে। কিন্তু সে জ্ঞান সে অর্জন করেছে ভেষজ-শাস্ত্র থেকে, ‘জ্ঞানের বিজ্ঞান’ থেকে নয়; যদি সে সঙ্গীতে সংগতির জ্ঞান পেয়ে থাকে, তাকেও অর্জন করেছে সঙ্গীতশাস্ত্র থেকে, ‘জ্ঞানের বিজ্ঞান’ থেকে নয়; কিংবা নির্মাণকৌশলকেও নির্মাণকলা থেকেই অর্জন করেছে। অর্থাৎ এ-সমস্ত বিদ্যার কোনোটিকেই সে জ্ঞান বা সংযম থেকে লাভ করে নি। ব্যক্তির অপরাপর বিদ্যা সম্পর্কেও একথা সত্য।
স্পষ্টতই একথা সত্য।
কাজেই ‘জ্ঞান’ যাকে তুমি শুধু ‘জ্ঞানের জ্ঞান’ বা ‘বিজ্ঞানের বিজ্ঞান’ বল, সে কি করে ব্যক্তিকে শিখিয়ে দিতে সক্ষম হবে যে, স্বাস্থ্য সম্পর্কে বা নির্মাণকলা সম্পর্কে তার জ্ঞান রয়েছে?
না, জ্ঞানের পক্ষে তা সম্ভব নয়।
কাজে কাজেই যে জ্ঞানী এই সমস্ত বিশেষ বিদ্যা সম্পর্কে অজ্ঞ সে ‘শুধু জানে এই কথাটি ব্যতীত অপর কী সে জানে, তা সে জানে না।
সে কথা ঠিক।
সুতরাং দেখা যাচ্ছে, জ্ঞান বা জ্ঞানী হওয়ার অর্থ এই নয় যে, যা আমরা জানি বা জানিনে তার জ্ঞান; জ্ঞানের অর্থ শুধু এই অবয়বহীন বোধ যে আমরা জানি বা জানিনে।
সেই অনুমানই আমাদের গ্রহণ করতে হচ্ছে।
তা হলে শুধু এই জ্ঞান যার আছে তার পক্ষে জ্ঞানের প্রতারককে যাচাই করা তো সম্ভব নয়। জ্ঞানের প্রতারক যে জ্ঞানের ভান করছে, তা যথার্থ কিংবা যথার্থ নয় তাকে নির্ধারণ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তোমার জ্ঞানী’ শুধু এতটুকু জানবে যে, এই ব্যক্তির কোনো প্রকারের জ্ঞান রয়েছে; কিন্তু তার নিজের জ্ঞান সেই জ্ঞানের প্রকৃতি নির্ধারণে মোটেই সাহায্য করতে সক্ষম হবে না।
এই বুঝতে পারছি।
আমাদের ‘জ্ঞানীর’ পক্ষে চিকিৎসার ক্ষেত্রে হাতুড়ে এবং যথার্থ চিকিৎসকের পার্থক্যও নির্ধারণ করা সম্ভব হবে না; জ্ঞানের অপর কোনো ক্ষেত্রেও সত্যিকার জ্ঞানী এবং প্রবঞ্চনাকারীর পার্থক্য সে বুঝতে সক্ষম হবে না। বিষয়টিকে আরো নির্দিষ্টভাবে দেখা যাক : আমাদের জ্ঞানী যদি হাতুড়ে এবং প্রকৃত চিকিৎসকের পার্থক্য নিরূপণ করার প্রয়াসও পায়, তা হলে এ ব্যাপারে কী পদ্ধতিতে সে অগ্রসর হবে? আমাদের ‘জ্ঞানী’ তো এই বিশেষ ব্যক্তির সাথে চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করতে সক্ষম হবে না; (কেননা সে শুধুই জানে, কিন্তু ‘বিশেষ কিছু’ জানে না)। আবার চিকিৎসকের পক্ষেও চিকিৎসাবিদ্যা ব্যতীত অপর কিছু বুঝতে পারা সম্ভব নয়।
ঠিকই।
কেননা ‘বিজ্ঞান’ সম্পর্কেও চিকিৎসাবিদ অজ্ঞ। ‘বিজ্ঞানকে’ বিশুদ্ধ জ্ঞানের আওতাভুক্ত বলে দাবি করা হয়েছে। তাই নয় কি?
তাই বটে।
আবার ভেষজের বিষয়টিও তো বিজ্ঞান। তা হলে দাঁড়ায় যে, যেহেতু ভেষজ হচ্ছে বিজ্ঞান সেজন্য চিকিৎসকের পক্ষেও চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে জানা সম্ভব নয়।
তাই তো দেখছি।
তা হলে আমাদের আলোচ্য ‘জ্ঞানী’ চিকিৎসকের যে-কোনো এক প্রকার জ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক বিদ্যা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কেননা, জ্ঞানের প্রকৃতি জানার জন্য প্রথম প্রশ্নই তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে। বিষয়টি কী? কারণ, বিজ্ঞানে পার্থক্য নির্দিষ্ট হয় বিষয়ের চরিত্র দ্বারা, শুধু তার বিজ্ঞান হওয়ার দ্বারা নয়। একথা কি তুমি ঠিক মনে কর না, ক্রিটিয়াস?
অবশ্যই ঠিক।
এ জন্যেই অন্যান্য বিজ্ঞানের সাথে ভেষজ-বিজ্ঞানের পার্থক্য এই যে, ভেষজ-বিজ্ঞান আরাম ও ব্যারামের বিজ্ঞান।
ঠিকই।
কাজেই কেউ যদি ভেষজবিদ্যার প্রকৃতি বুঝার প্রয়াশ পায়, তা হলে তাকে যে কোনো সম্পর্কহীন বিষয় নিয়ে অনুসন্ধান করলে চলবে না, তাকে অবশ্যই সুস্থতা এবং অসুস্থতার বিষয় নিয়েই অনুসন্ধান চালাতে হবে।
অবশ্যই
এবং চিকিৎসককে যদি কেউ যাচাই করতে চায়, তা হলে চিকিৎসক হিসাবেই তাকে যাচাই করতে হবে।
হ্যাঁ।
তাকে বিচার করতে হবে, চিকিৎসক যা বলে কিংবা করে সুস্থতা এবং অসুস্থতার ক্ষেত্রে তা সত্য কি মিথ্যা।
ঠিক।
কিন্তু যে “জ্ঞানীর’ ভেষজবিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞান নেই, তার পক্ষে কি সুস্থতা-অসুস্থতা কোনোটিরই প্রকৃতি জানা সম্ভব?
না, সম্ভব নয়।
চিকিৎসক ব্যতীত অপর কারো পক্ষেই এক জ্ঞান থাকা সম্ভব নয়। কাজেই আমাদের জ্ঞানী মানুষেরও এই জ্ঞান থাকা সম্ভব নয়। সুস্থতা-অসুস্থতার জ্ঞান পেতে হলে তাকে অবশ্যই চিকিৎসক এবং জ্ঞানী উভয়ই হতে হবে।
খুবই সত্য।
কাজে কাজেই দেখতে পাচ্ছ যে, সংযম বা জ্ঞানকে যদি মাত্র বিজ্ঞানের বিজ্ঞান এবং অজ্ঞান ও অবিজ্ঞানের কথা বল, তা হলে এরূপ সংযমী বা জ্ঞানী কোনো প্রতারক চিকিৎসককে খাঁটি চিকিৎসক থেকে পৃথক করতে সক্ষম হবে না। জ্ঞানের অপর যে কোননা ক্ষেত্রে প্রতারক ও খাঁটির পার্থক্য বুঝতে সে অক্ষম।
এটি এবার পরিষ্কারই দেখা যাচ্ছে।
এই যদি জ্ঞান হয়, তা হলে জ্ঞান ও সংযমের আর মূল্য কী? আমরা প্রথমে যেরূপ ভেবেছিলাম, প্রকৃতপক্ষে সেভাবে জ্ঞানী মানুষ যদি কী সে জানে এবং কী জানে না তাকে জানতে পারত এবং অপরের মধ্যেও জানা, অজানার পার্থক্য নির্দিষ্ট করতে সক্ষম হতো তা হলে এরূপ জ্ঞানী হওয়ার যথেষ্ট সার্থকতাই থাকত। কেননা, তা হলে এই জ্ঞানের সাহায্যে আমরা ভ্রান্তিশূন্য জীবনযাপন করতে সক্ষম হতাম, নিজেকে এবং অপরকে ভ্রান্তিহীনভাবে পরিচালিত করতে পারতাম; যা আমরা জানিনে, জানা এবং করার অহমিকা না দেখিয়ে যে জানে তাকেই খুঁজে বার করে তার উপরই সে কাজ সম্পাদনের ভার ন্যস্ত করে আশ্বস্ত হতাম। পরিচালনার ক্ষেত্রেও যার যে জ্ঞান আছে। তাকে শুধু সে কাজ করারই অনুমতি দিতাম; কেননা তাকেই সে উত্তমরূপে সমাধা করতে পারে। এবং এরূপ জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত পরিবার কিংবা রাষ্ট্রে অবশ্যই সুশৃঙ্খলা বিরাজ করত। সত্য সেখানে পথ-প্রদর্শকের কাজ করত, ভ্রান্তি পরিহার করা সম্ভব হত; মানুষের কর্তব্যকর্ম সু-সাধিত হতে; মানুষ সুখী হতো। জ্ঞানের সার্থকতা তো এ সমস্তই। তাই নয় কি ক্রিটিয়াস? যা আমাদের জানা এবং যা অজানা তাকে জানতে পারাই তো জ্ঞান?
নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।
কিন্তু এবার তুমি দেখতে পাচ্ছ, এরূপ বিজ্ঞানের সাক্ষাৎ আমরা কোথাও পাইনে।
হ্যাঁ, তাই তো দেখছি।
তা হলে এস আমরা নূতন আলোকে জ্ঞানকে দেখবার চেষ্টা করি। নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে জ্ঞানকে আমরা পুনরায় জানা-অজানার জ্ঞান হিসাবে বিচার করব। তার সার্থকতার দাবি কতখানি ঠিক তাকেও আমরা পরীক্ষা করব। আমরা বলেছি যে জানা অজানার জ্ঞানে জ্ঞানী অবশ্যই তার শিক্ষণীয়কে সহজতরভাবে শিখতে সক্ষম হবে; ব্যক্তির সম্পর্কে তার জ্ঞান এবং জ্ঞানের সাধারণ নীতি নিয়ে যে বিজ্ঞান তার পরিচয় ব্যক্তির পরিচয়কেও অধিকতর সম্যক করে তুলবে। তার আপন জ্ঞানের আলোকে অপরের জ্ঞানকেও সে বিচার করতে সক্ষম হবে। কিন্তু যে অনুসন্ধানীর এরূপ জ্ঞান নেই, তার অন্তর্দৃষ্টি হবে দুর্বল এবং ক্ষীণ। বস্তুত আমাদের পুরাতন বিশ্লেষণ অনুযায়ী এই সার্থকতাই তো আমরা বিজ্ঞান থেকে লাভ করতে চাই, তাই নয় কি ক্রিটিয়াস? এর অধিক দাবি করার অর্থ হচ্ছে ‘জ্ঞানের মধ্যে যা নেই তাকেই খুঁজে বার করার চেষ্টা করা।
হ্যাঁ, তাতে অধিক পাওয়ারই চেষ্টা করা হবে।
হ্যাঁ, তাই। এবং আমরা এযাবৎ নিষ্ফলভাবে সে চেষ্টাই করে এসেছি। কারণ, জ্ঞানকে যদি পূর্বের মতোই মনে করা হয়, তা হলে তা থেকে অবাঞ্ছিত পরিণামই দেখা দেবে। ধর যদি বিজ্ঞানের বিজ্ঞান বলে কোনো বিজ্ঞান থাকে এবং যদি প্রথম প্রতিপাদ্যের ন্যায় মনে করি যে, জ্ঞান হচ্ছে, যা আমরা জানি এবং যা জানিনে তার জ্ঞান’ তা হলে নূতন পরীক্ষায় আমরা দেখতে পাব যে এমন জ্ঞানের সত্যিকার কোনো সার্থকতা নেই। কারণ অবয়বহীন এমন জ্ঞান দ্বারা আমাদের পূর্বের সিদ্ধান্তকে প্রত্যাহার করা আবশ্যক। আমরা পূর্বে ভ্রান্তভাবেই মনে করেছি যে, এই জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত পরিবার ও রাষ্ট্রে সুশৃঙ্খল বিরাজ করবে।
তুমি তোমরা পূর্বের মত প্রত্যাহার করছ?
হ্যাঁ, তাই। কারণ অত সহজে আমাদের এ অনুমান করা সংগত হয় নি যে, ব্যক্তি যদি আপন আপন জ্ঞান অনুসারে নিজ কর্তব্য সম্পাদন করে এবং যা সে জানে না তার সম্পাদনভার যে জানে তার উপর অর্পণ করে তা হলেই মানবজাতি বিরাটভাবে উপকৃত হবে।
কেন, তেমন অনুমান কি সঠিক নয়?
না, এখন আমি সে অনুমানকে সঠিক মনে করিনে।
সক্রেটিস, কী অদ্ভুত তোমার যুক্তি-পদ্ধতি।
মিশর দেশের সারমেয়র নামে আমি শপথ করে বলতে পারি, ক্রিটিয়াস, এ ব্যাপারে তোমার সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত। এবং আমি যখন খানিকপূর্বে দুঃখজনক পরিণামের কথা বলছিলাম তখন আমার একথাই মনে হচ্ছিল। আমার তখনি বোধ হচ্ছিল, আমরা ভ্ৰান্তপথে অগ্রসর হচ্ছি। কেননা যত সহজেই জ্ঞানকে আমরা উল্লিখিতভাবে স্বীকার করিনে কেন, আমাদের জীবনে এ জ্ঞানের সার্থকতা কোথায়?
ক্রিটিয়াস বলে উঠল : দোহাই সক্রেটিস, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছিনে। তুমি কি দয়া করে স্পষ্টভাবে আমাকে বুঝিয়ে বলবে, কী তুমি বুঝাতে চাচ্ছ?
এ ব্যাপারেও আমি তোমার সাথে একমত। আমি জানি যা বলেছি, তা অর্থহীন জাল বুননি বোধ হচ্ছে। তবু বুদ্ধির প্রতি সততা রেখে কেউ কি নিজের মনের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে অস্বীকার করতে পারে?
তোমার এ মনোভাবটি আমি প্রশংসা করি সক্রিটিস।
তা হলে ক্রিটিয়াস, তুমি আমার স্বপ্নকথা শ্রবণ কর। এটা আমার অলীক কল্পনা। কিনা তা আমি জানিনে। তবু তুমি শ্রবণ কর। মনে কর যে সংজ্ঞা আমরা দিয়েছি, জ্ঞান তাই। এবং জ্ঞান দ্বারাই আমরা সবাই চালিত হই। তা হলে ব্যক্তিমাত্রেরই প্রত্যেকটি কার্য বিজ্ঞান বা কলার নীতি অনুসারেই সম্পাদিত হবে। কাজেই যে যান পরিচালক নয় সে নিজেকে যান-পরিচালক বলে দাবি করতে পারে না এবং যে চিকিৎসক নয় বা সামরিক বাহিনীর অধিনায়ক নয় সেও নিজেকে চিকিৎসক বা অধিনায়ক বলে নিজেকে দাবি করতে পারবে না। অর্থাৎ প্রতারণার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। কোনো প্রতারক আর আমাদের প্রবঞ্চনা করতে সক্ষম হবে না। আমাদের জনস্বাস্থ্য রক্ষিত হবে, আমাদের সমুদ্রযাত্রায় এবং যুদ্ধক্ষেত্রেও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ঘটবে; কারিগরবৃন্দ সততার সাথে আপন আপন কর্তব্য সাধন করবে এবং আমাদের পরিচ্ছদ, পাদুকা এবং অপরাপর আসবাব ও যন্ত্রাদি সুকৌশলে নির্মিত হবে। শুধু এ পর্যন্ত কেন? এস আমরা আর একটু অগ্রসর হই। ভবিষ্যদ্বক্তার স্থলে সত্যকার ভবিষ্যদ্বক্তার প্রতিষ্ঠা হবে। একথা স্বীকার করা যায় যে, এরূপ হলে মানবজাতি জ্ঞান দ্বারাই পরিচালিত হবে। প্রজ্ঞা প্রহরীর ন্যায় অজ্ঞতাকে মানুষের জীবন থেকে দূরে ঠেকিয়ে রাখবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে-প্রশ্নটির মীমাংসা আমরা এখনো করতে পারি নি সে হচ্ছে এই যে : মানুষ যদি প্রজ্ঞা দ্বারা চালিত হয় তা হলেও সে কি সত্যকারভাবে সুখী হতে পারবে?
ক্রিটিয়াস বলল : তথাপি আমার ধারণা যে, জ্ঞানকে পরিত্যাগ করে সুখের মুকুট আমরা কোথাও খুঁজে পাব না।
কিন্তু কিসের জ্ঞান, ক্রিটিয়াস? তুমি শুধু এই ছোট্ট প্রশ্নটির জবাব দাও। কিসের জ্ঞান? পাদুকা প্রস্তুত করার জ্ঞান?
কি যে বল!
অথবা অলঙ্কার নির্মাণের?
তাও নয়।
অথবা পশম, কাষ্ঠ বা এই জাতীয় অপর কোনো কাজের জ্ঞান?
না, আমি তা মনে করিনে।
তা হলে আর বলা চলে না যে, জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হলেই মানুষ সুখী হবে। উপরে যাদের কথা উল্লেখ করা হলো তারা তো জ্ঞান অনুযায়ী আপন আপন কার্য সম্পন্ন করে। তথাপি তুমি তো তাদের সুখী বলতে চাও না। আমার মনে হচ্ছে তুমি সুখকে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখতে চাচ্ছ। হয়তো তুমি বলতে চাচ্ছ যে, ভবিষ্যদ্বক্তার ন্যায় যাদের ভবিষ্যকালের জ্ঞান আছে, তারাই সুখী। তুমি কি এরূপ কোনো অংশকেই সুখী বলতে চাচ্ছ, ক্রিটিয়াস?
হ্যাঁ, আমি অবশ্য এরূপ লোককে ভেবেই বলেছি। কিন্তু তা ছাড়াও তো সুখী ব্যক্তি রয়েছে।
হ্যাঁ আছে। সে কেবল তেমন ব্যক্তি যে ভূত-ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান সম্বন্ধে শুধু নয়, . সবকিছুই যে জানে, তেমন ব্যক্তিকেই তুমি সর্বজ্ঞানী ও সর্বসুখী বলে ভাবতে পার।
হ্যাঁ, এরূপ মানুষই সর্বজ্ঞানী ও সর্বসুখী।
তবু তুমি আর একটি কথা আমায় বুঝিয়ে বল, ক্রিটিয়াস। এমন ব্যক্তির সবকিছুর জ্ঞান আছে সত্য। কিন্তু কোন বিশেষ জ্ঞান তাকে বেশি সুখী করে? অথবা তুমি কি মনে কর যে, সব জ্ঞানই তাকে সমানভাবে সুখী করে?
না, সব জ্ঞান নিশ্চয়ই তাকে সমভাবে সুখী করে না।
তা হলে কোন বিষয়ের জ্ঞান বেশি সুখী করতে পারে? সেকি ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের জ্ঞান? না, সতরঞ্চ না দাবা খেলার জ্ঞান?
সতরঞ্চ খেলা তো অর্থহীন।
তা হলে গণনের জ্ঞান?
না।
দেহকে সুস্থ রাখার জ্ঞান? একথা সত্যের কিছুটা নিকটবর্তী।
একথা যদি সত্যের কিছুটা নিকটবর্তী হয় তা হলে কোন জ্ঞান সত্যের একেবারে নিকটবর্তী : অর্থাৎ কোন জ্ঞান আর আংশিক নয়, পরিপূর্ণভাবে সত্য।
যে জ্ঞান দ্বারা আমরা শুভ-অশুভকে অনুভব করতে সক্ষম হই।
কী অদ্ভুত। সক্রেটিস, তুমি আমাকে চক্রাকারে ঘুরিয়ে চলেছ। অথচ এই কথাটিই তুমি এতক্ষণ অবধি আমার নিকট থেকে গোপন করে রেখেছ যে, শুভ-অশুভের জ্ঞান বই অপর কোনো জ্ঞানই মানবজীবনকে সঠিকভাবে পরিচালিত বা সম্পূর্ণরূপে সুখী করে তোলে না। তথাপি আমি বলি, ক্রিটিয়াস, শুভ-অশুভের জ্ঞানকেও যদি আমরা অস্বীকার করি, তা হলেও দেহের উপর ঔষধের মঙ্গলকর ক্রিয়া কি বন্ধ হয়ে যাবে? পাদুকা প্রস্তুতকারী কারিগর কি পাদুকা প্রস্তুতে অসমর্থ হয়ে পড়বে, বয়নশিল্পী কি আপন শিল্পদক্ষতাকে বিস্মৃত হবে, নৌযান পরিচালক কি সমুদ্রবক্ষে এবং সেনাধিপতি যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের নিরাপত্তা রক্ষায় ব্যর্থ হবে?
না, তা তো নয়ই।
তা হলেও তুমি হয়তো বলবে, শুভ-অশুভের বিজ্ঞান ব্যতীত এ সমস্ত কাজের কোনোটিই সুসম্পন্ন হবে না?
আমার তাই মনে হয়।
কিন্তু শুভ-অশুভের বিজ্ঞান কি জ্ঞান বা সংযমের বিজ্ঞান? তা তো নয়। তোমার শুভ অশুভের বিজ্ঞান হচ্ছে শুধু উপকারিতার বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের বিজ্ঞান বা অজানার বিজ্ঞান নয়। সুতরাং শুভ-অশুভের বিজ্ঞানই যদি সার্থকতার বিজ্ঞান হয় তা হলে জ্ঞান বা সংযমের বিজ্ঞান কোনো সার্থকতার বিজ্ঞান নয়।
ক্রিটিয়াস আমার এ সিদ্ধান্তে আপত্তি জানিয়ে বলল : কেন? প্রজ্ঞার বিজ্ঞান অসার্থকতার বিজ্ঞান কেন হবে? কেননা জ্ঞানকে আমরা বিজ্ঞানের বিজ্ঞান বলেছি এবং অপর সমস্ত বিজ্ঞানের উপর তার প্রভাবের কথা স্বীকার করেছি। কাজেই শুভ-অশুভের বিজ্ঞানও প্রজ্ঞার বিজ্ঞানের প্রভাবাধীন বলে বিবেচিত হবে। এবং সেদিক দিয়ে, যেহেতু শুভ-অশুভের বিজ্ঞান হচ্ছে সার্থকতার বিজ্ঞান এবং যেহেতু সার্থকতার বিজ্ঞান প্রজ্ঞার বিজ্ঞানেরই অধীন সেজন্য প্রজ্ঞার বিজ্ঞানও সার্থকতারই বিজ্ঞান।
কিন্তু প্রজ্ঞা কি আমাদের স্বাস্থ্য দান করে? না, স্বাস্থ্য হচ্ছে ঔষধ প্রয়োগের ফল? ‘জ্ঞান’ কি অপর কোনো শিল্প-কৌশলের কাজ সমাধা করে দিতে পারে? আমরা কি বহু পূর্বেই দ্ব্যর্থহীনভাবে বলি নি যে, ‘প্রজ্ঞা’ হচ্ছে কেবল ‘জ্ঞান এবং অ-জ্ঞানের জ্ঞান’, অপর কিছু নয়।
সে তো ঠিক।
তা হলে একথাও ঠিক যে প্রজ্ঞা আমাদের সম্পদ সৃষ্টি করে না?
না, তা করে না।
স্বাস্থ্যরক্ষার কৌশলও ভিন্ন প্রকৃতির?
হ্যাঁ, অবশ্যই ভিন্ন প্রকৃতির।
তা ছাড়া, প্রিয় বন্ধু প্রজ্ঞার মাধ্যমে কোনো সুবিধা বা উপকার লাভ আমরা করি না। এ কার্য অপর একটি বিজ্ঞান সাধন করে একথা আমরা কিছু পূর্বেই বলেছি।
সে কথাও সত্য।
তা হলে যে-’প্রজ্ঞা’ কোনো সার্থকতা বহন করে আনে না তাকে তুমি সার্থকতার জ্ঞান কী করে বলবে?
না, তাও তো বলা চলে না।
তা হলে ক্রিটিয়াস তুমি এবার বুঝতে পারছ, কেন আমি জ্ঞান সম্পর্কে আমার নিজ জ্ঞানকে অস্বীকার করেছিলাম। জ্ঞান সম্পর্কে আমার অজ্ঞানতা অর্থাৎ আমার অক্ষমতা প্রকাশ যথার্থই হয়েছিল। কেননা, আমার আপন বিচার-ক্ষমতার উপর সামান্য আস্থা থাকলেও বলতে হয় যে, যাকে সর্বোত্তম বলা চলে সে নিশ্চয়ই সার্থকতাহীন বলে অনুভূত হতে পারে না। কিন্তু আমার অনুসন্ধান-ক্ষমতাও ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে : সংযম বা প্রজ্ঞা সত্যকারভাবে কাকে বলা হয় আমি তা নির্ধারণ করতে অক্ষম হয়েছি। অথচ একাধিক অভিমত আমরা প্রমাণের অপেক্ষা না রেখেই প্রকাশ করেছি। আমরা বলেছি : বিজ্ঞানের বিজ্ঞান আছে। যুক্তি বলেছে : না, তা সম্ভব নয়। আমরা বলেছি; এই বিজ্ঞান সব বিজ্ঞানের কার্যই সমাধা করে। যুক্তি বলেছে : এর কোনো প্রমাণ নেই। একথা বলার উদ্দেশ্য ছিল, আমরা প্রমাণ করতে চেয়েছি যে, জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞান ও অ-জ্ঞান উভয়ের জ্ঞান রাখে। অথচ যা অ-জ্ঞান’ তা যে কখনো জ্ঞান’ হতে পারে না অর্থাৎ যে ব্যক্তি যা জানে না তা সে অবশ্যই জানে না; সে না-জানাকে যে আমরা একই সাথে তার জানার অন্তর্ভুক্ত করতে পারিনে, যুক্তির এই সাধারণ নীতিকেও পরোয়া করি নি। কারণ, আমাদের মনে পূর্ব-কল্পিত এক বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে এক ব্যক্তির পক্ষে জানা এবং অ-জানা উভয়কে জানা সম্ভব। কিন্তু এরূপ চিন্তা করা অসংগতির চরম। আমাদের এত ইচ্ছামূলক স্বীকৃতি সত্ত্বেও প্রজ্ঞার’ সত্যতা আমাদের নিকট ধরা দিতে আদৌ সম্মত হলো না; এ সত্য এখনো আমাদের এড়িয়ে চলছে। আমাদের বিচার্য প্রশ্ন এখন এত জটিল ও হাস্যাস্পদ আকার গ্রহণ করেছে যে প্রতিপাদ্যের বিরোধী সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ সংযম বা জ্ঞানের যে সংজ্ঞাকে আমরা সর্বতোভাবে সঠিক মনে করেছিলাম সে সংজ্ঞার বিরোধী সত্যই প্রকট হয়ে উঠেছে। যা সার্থক ছিল তা এখন মূলত অসার্থক বলে অনুভূত হচ্ছে। এ পরিণতির জন্য ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনো খেদ নেই। আমার আফসোস, চারমিডিস, শুধু তোমার জন্য। আমার দুঃখ তোমার এরূপ কালিমাহীন দেহসৌষ্ঠব এবং আত্মার প্রজ্ঞা এবং সংযম থাকা সত্ত্বেও প্রজ্ঞা বা সংযম তোমার জন্য কোনো সার্থকতা বহন করে আনে না। অনুতাপ এজন্যও যে প্রেসবাসীদের নিকট হতে অতিশয় পরিশ্রম সহকারে যে-বিদ্যার জন্য জাদুমন্ত্রকে আয়ত্ত করে আনলাম সে বিদ্যাই মূল্যহীন? তাই আত্মধিক্কারের সাথে বরঞ্চ আমি বলি; কোথাও কোনো ত্রুটি ঘটেছে। এবং সে ক্রটি আমার অক্ষমতারই ত্রুটি। কারণ প্রজ্ঞা ও সংযম তো অবশ্যই মঙ্গলকর গুণবিশেষ। চারমিডিস, তুমি যদি যথার্থই এ গুণের অধিকরী হয়ে থাক, তা হলে তুমি অবশ্যই সুখী। কাজে কাজেই আত্মপরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে তুমি বিচার করে দেখ যথার্থই তুমি এ গুণে গুণী কিনা এবং যে জাদুমন্ত্রের উল্লেখ আমি করেছি সে জাদুমন্ত্র ব্যতিরেকেই তুমি সুস্থ হতে পার কিনা? তা যদি সম্ভব হয়, তা হলে বরঞ্চ আমাকে তুমি মূর্খ বলেই জেনো এবং নিজের ওপর এই বিশ্বাস রেখো যে, যত অধিক তুমি সংযমে সংযমী এবং জ্ঞানী হয়ে উঠবে, তত অধিক তুমি সুখী হবে।
চারমিডিস বলল : প্রাজ্ঞ, একথা আমি নিশ্চয় করে জানিনে জ্ঞান ও সংযমের এই গুণ আমার মধ্যে আছে কিংবা নাই। কেননা আপনি এবং ভ্রাতা ক্রিটিয়াস যে গুণের রূপ নির্ণয়ে পরাজয় স্বীকার করেছেন সে গুণে গুণান্বিত বলে দাবি করা আমার পক্ষে শোভনীয় নয়। কিন্তু আপনাদের পরাজয় স্বীকারকে আমি গ্রহণ করতে পারিনে। তাই আপনার জাদুমন্ত্র গ্রহণের আবশ্যকতা আমি অনুভব করি। বস্তুত প্রতিদিনই যেন আপনার মন্ত্রে বিমোহিত হবার সৌভাগ্য আমি লাভ করতে পারি।
ক্রিটিয়াস বলল : অতি উত্তম চারমিডিস। সক্রেটিসের মন্ত্রদানে তুমি যদি সম্মত হও, যদি না কখনো তুমি তাকে পরিত্যাগ কর তা হলে অবশ্যই তোমার সংযমের প্রমাণ মিলবে।
ক্রিটিয়াস, আপনি আমার অভিভাবক। আপনার আদেশ শিরোধার্য। আপনি বিশ্বাস করুন, আমি প্রাজ্ঞ সক্রেটিসকে অনুসরণ করা থেকে কখনো বিরত হবো না।
আনন্দের সাথে আমি সেই আদেশ দিচ্ছি, চারমিডিস।
আপনার আদেশ গ্রহণ করে অদ্য হতেই আমি মনীষী সক্রেটিসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলাম।
আমি বলে উঠলাম : কি হে আমার বিরুদ্ধে তোমরা দুভাই মিলে কি ষড়যন্ত্র তৈরি করে তুলছ?
ষড়যন্ত্র সাধন হয়ে গেছে, প্রাজ্ঞ! তৈরি করার অবস্থা আমরা অতিক্রম করে এসেছি। তরুণ! তোমরা আমার কি কোনো বিচার পর্যন্ত না করে জবরদস্তি প্রয়োগ করবে।
রসিক প্রাজ্ঞ। ভ্রাতা ক্রিটিয়াসের আদেশ আমার শিরোধার্য। তিনি তেমন আদেশ দিলে কি আমি তা পালন করব না? আপনি আমায় বলে দিন।
কিন্তু বৎস! তোমার যেরূপ দৃঢ়তা তাতে আমার বিষয় বিবেচনার পর্যায় তো অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তোমার দাবি যে অপ্রতিরোধ্য।
মন্ত্রদাতা! তা হলে আমায় আপনি গ্রহণ করুন।
আমি তোমাকে গ্রহণ করলাম, বৎস।