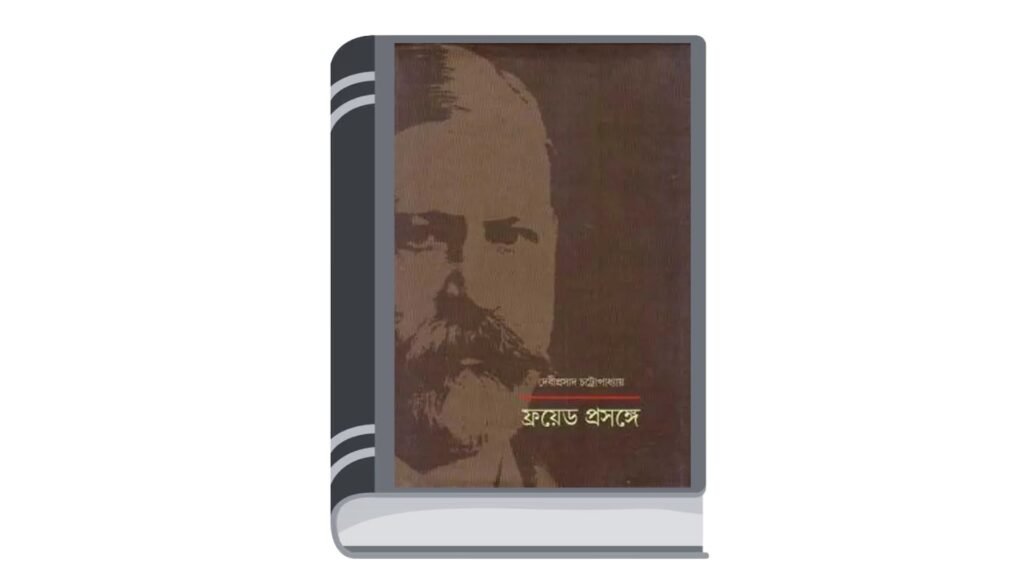৪. প্রতিবন্ধ
ফ্রয়েডীয় কলাকৌশলের আর একটি খুব জরুরী কথা হলো প্রতিবন্ধের কথা: চিকিৎসকের বিরুদ্ধে, চিকিৎসা-পদ্ধতির বিরুদ্ধে, রোগীর তরফ থেকে অনেক রকম স্থূল ও সূক্ষ্ম ওজর-আপত্তি। রোগী যেন পণ করে বসেছে, রোগমুক্তিকে যেমন করেই হোক রুখতে হবে। ফ্রয়েড বলেছেন, আপাতত অদ্ভুত মনে হলেও এর সুনির্দিষ্ট কারণ রয়েছে। প্রথমত, রোগলক্ষণ থেকে রোগী একরকম কাল্পনিক সুখ পান, রোগমুক্তি মানেই সেই সুখের সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত হবার ভয়। উপমা দিয়ে ফ্রয়েড বলেন, কোনো কোনো ভিখিরী তো হাতে ঘা পোষে: ঘা দেখিয়েই ভিক্ষে জোটে, তাই ওর ঘায়ের চিকিৎসা করতে গেলে ভিখিরী বাধা দেবে বই কি! (১২) মনোবিকার থেকেও যেন একরকম ভিক্ষে পাওয়া যায়, ফ্রয়েড তার নাম দেন রোগ-থেকে-পাওয়া মুনাফা। কেবল মনে রাখতে হবে এই মুনাফাটা রোগীর সজ্ঞানে নয়। এর খবরটা রোগী নিজেই নিজের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখেন। দ্বিতীয়ত, ফ্রয়েডের মতে এখানে আরো একটা কথা আছে। তাঁর কলাকৌশলের উদ্দেশ্য হলো রোগীর নিজের চেষ্টার একেবারে বিপরীত : রোগী নিজের কাছ থেকেও যে-কথা গোপন রাখতে চান সেই কথাই প্রকাশ করবার উদ্দেশ্য তাঁর কলাকৌশলের। তাই প্রতিবন্ধটা স্বাভাবিকই।
অবশ্যই ফ্রয়েড বলেন, এই প্রতিবন্ধের পরিচয় শুধুই চিকিৎসা-প্রসঙ্গে নয়। এর একটা বৃহত্তর সামাজিক সংস্করণ আছে। তার মানে, সাধারণত সামাজিকভাবে ফ্রয়েডবাদের বিরুদ্ধে যে-আপত্তি তা ওই প্রতিবন্ধেরই পরিবর্ধিত বিকাশমাত্র। (১৩)
এবং, প্রতিবন্ধ নিয়ে আলোচনা করবার সময় তাঁর এই পরিবর্ধিত সামাজিক বিকাশটার বিশ্লেষণ থেকেই শুরু করার সুবিধে। কেননা, বন্ধ ঘরের আধো অন্ধকারে ব্যক্তিবিশেষের ব্যবহারের মধ্যে যে-কথাটাকে রহস্যঘন করে তোলবার সুযোগ, বৃহত্তর সামাজিক জীবনেও দিনের আলোয় তারই যে-পুনঃপ্রকাশ, তার উপর রহস্যের জাল বোনবার সুযোগ অনেক কম। অর্থাৎ আলোচনার সুযোগ-সুবিধে অনেক বেশি। তাই প্রতিবন্ধের এই সমাজ-রূপটা নিয়েই আলোচনা শুরু করা যাক।
ফ্রয়েডের মতে, তাঁর আবিষ্কারটুকুকে ভুলে থাকতে পারলেই মানবসমাজের নিশ্চিন্ত আরাম। মনোবিকারের রোগী রোগ-মুনাফা নামের যে-রকম আরাম পায় সেই রকমই। কেননা, তিনি এমন কতকগুলি কথা আবিষ্কার করেছেন বলে দাবি করেন, যা শুধুই মানবমনের আত্মাভিমানকেই পীড়িত করে না, এমন কি মানবসমাজের বনিয়াদটুকুকেও সংকটাপন্ন করে তোলে। আত্মাভিমানটা পীড়িত হবার কথা কেন? তার কারণ, ফ্রয়েড বলছেন, মানুষের চিরন্তন অভিমান হলো সচেতন কীর্তির অভিমান; অথচ তাঁর আবিষ্কার প্রতিপন্ন করছে এই সব সচেতন কীর্তির পিছনে রয়েছে কতকগুলি অন্ধ, অচেতন এবং সামাজিকভাবে নিকৃষ্ট বাসনার তাগিদ। মানুষের অভিমান এতে আহত হবে না? ফ্রয়েড বলছেন, বিজ্ঞানের ইতিহাসে মানুষের আত্মাভিমান এর আগে আর দুবার এই রকম ভাবে আহত হয়েছিল। এক, কোপার্নিকাস যখন প্রমাণ করলেন, আমাদের এই পৃথিবী সত্যিই সৌরজগতের কেন্দ্র নয়। আর দুই, ডারউইন যখন প্রমাণ করলেন, আমাদের এই প্রজাতি আসলে একরকম বনমানুষের বংশধর। (১৪) আর, মানুষের আত্মাভিমান অমন সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছিল বলেই এই দুটি মতবাদের বিরুদ্ধেও দেখা দিয়েছিল দারুণ সামাজিক প্রতিবন্ধ!
কিন্তু ফ্রয়েডীয় মতবাদের দরুন মানবসমাজের বনিয়াদটা সংকটাপন্ন হয়ে পড়বে কেন? তার কারণ ফ্রয়েড বলেছেন, সমাজ-সভ্যতা বলে মানুষ যা-কিছুই গড়ে তুলেছে তাই তার নিজের যৌন-চরিতার্থতাকে খর্ব করে, সঙ্কুচিত করে গড়ে তোলে। যৌন তাগিদটাই যেন ইন্ধন, এই ইন্ধন জোগান দেওয়া গিয়েছে বলেই সভ্যতার বহ্নি এমন দীপ্ত কিরণে ইতিহাসকে উদ্ভাসিত করতে পেরেছে। মানুষের সভ্যতা তো এমনি গড়ে ওঠেনি, আত্মত্যাগের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়। ফ্রয়েড মনে করেন, সভ্যতা যে বিরাট আত্মত্যাগ মানুষের কাছ থেকে দাবি করে তার অনুপাতে সভ্যতার প্রতিদানটা যৎসামান্যই। (১৫) অর্থাৎ, আত্মত্যাগটা অনেকাংশে অহেতুক, অর্থহীন। আর এই কথাটা মানুষ যদি স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে শেখে তাহলে সভ্যতার বনিয়াদটুকু কেঁপে উঠবে না কি? সভ্যতার তরফ থেকে এই মতবাদের বিরুদ্ধে অভিযানটা তাই।
অবশ্যই, ফ্রয়েডের মতে মানুষের আত্মাভিমান আর সমাজ-সভ্যতা সব কিছুই ইতিহাস-উত্তীর্ণ শাশ্বত ও সনাতন ব্যাপার। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে এর ইতরবিশেষে যদিই বা কোনো তফাত দেখা দেয় তা হলেও সে-তফাত মৌলিক নয়। অর্থাৎ বাইরের দিকে এই রদবদল যাই হোক না কেন ভিতরের চেহারাটা বরাবর একই রকম। তার মানে ফ্রয়েডের চেতনায় ইতিহাসবোধ—এর স্থান নেই।
এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, ফ্রয়েড যখন প্রথম তাঁর মতবাদ পেশ করেন তখন এই মতবাদের বিরুদ্ধে তীব্র সামাজিক নিন্দা ও আন্দোলন দেখা দিয়েছিলো। বিরুদ্ধ পরিবেশের সঙ্গে অনেকদিন ধরে অনেকভাবে তাঁকে যুঝতে হয়েছে। (১৬) কিন্তু তার আসল কারণ যদি এই হতো যে তাঁর মতবাদ মানুষের আত্মাভিমান আহত করেছে, সংকটাপন্ন করে তুলেছে সভ্যতার বনিয়াদ, তাহলে হঠাৎ আজকের দিনে ব্যাপারটা এমন আশ্চর্যভাবে বদলে গেলো কেন? ইংরেজ এবং বিশেষ করে মার্কিন মুলুকের কথা ভেবে দেখুন: সাইকোএ্যানালিসিস্ নিয়ে কী প্রবল প্রচণ্ড উৎসাহ! কী অজস্র অর্থব্যয়। গল্প-উপন্যাস, দৈনিক-সাপ্তাহিক থেকে শুরু করে সিনেমা-টেলিভিশন পর্যন্ত আধুনিক জগতের যতো রকম প্রচার-মাধ্যম আছে তার সাহায্যে সাইকোএ্যানাসিলিসের প্রচণ্ড প্রচার। (১৭) এই প্রচার-ব্যবস্থার পরিচয় খুঁটিয়ে দিতে গেলে অনেকখানি জায়গা যাবে। আধুনিক মার্কিন সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে যাঁর সামান্যতম পরিচয়ও আছে তিনিই জানেন আজকের দিনে ওদেশে সাইকোএ্যানালিসিস নিয়ে কী ধুমধাম। ফ্রয়েড তাঁর জীবদ্দশায় একবার আক্ষেপ করে বলেছিলেন, আধুনিক সভ্যজীবন মানুষের উপর অসহ্য বোঝা চাপিয়েছে। এ-সম্বন্ধে একটা সংশোধন-ব্যবস্থার প্রয়োজন, এবং হয়তো কোনো একদিন সত্যিই কোনো কোটিপতি মার্কিন দাতা কোটি কোটি টাকা দান করে সমাজ-কর্মীর দলকে সাইকোএ্যানালিটিক্যাল্ কলাকৌশলে দীক্ষিত করে তুলবেন, আধুনিক জীবন যে-বিকারগ্রস্ত অবস্থা সৃষ্টি করেছে, তার সঙ্গে এঁরা সঙ্কটত্রাণ ফৌজের মতো লড়াই করতে পারবেন। (১৮) আজকের দিনে ফ্রয়েড যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে তিনি নিশ্চিতই দেখতে পেতেন কোনো নির্দিষ্ট মার্কিন দাতা মহারাজের প্রত্যক্ষ দান হিসেবে না হলেও মার্কিন মুল্লুকে সত্যিই সাইকোএ্যানালিসিসের পিছনে কোটি কোটি টাকা খরচ করবার আয়োজন। রাজনীতির ঘোরপ্যাঁচ কিন্তু এমনই পরিহাস-রসিক যে এই উৎসাহের উদ্দেশ্যটা আধুনিক জীবনের গ্লানিকে হালকা করা নয়, আধুনিক সমাজ ব্যবস্থাকে—অতএব এই গ্লানিকেই টিকিয়ে রাখবার ব্যর্থ প্রয়াস।
তাহলে ফ্রয়েড যে ব্যাপারটাকে সাইকোএ্যানালিসিসের বিরুদ্ধে মূল প্রতিবন্ধের বৃহৎ সামাজিক বিকাশ বলে বর্ণনা করছেন সেইটের কী হলো? সত্যিই কি কোনো রকম আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ ওই প্রতিবন্ধটার জাত-বদল করে ওকে অবৈধ উৎসাহে পরিণত করেছে? কিন্তু তা তো আর বাস্তবিক সম্ভব নয়। যে-মতবাদ ফ্রয়েডের মতে মানুষের আত্মাভিমানকে নির্মমভাবে আহত করে, আজকের ক্ষয়িষ্ণু পৃথিবীতে সেই মতবাদই মানুষের কাছে এমন প্রিয় হয়ে উঠলো কী করে? যে-মতবাদ ফ্রয়েডের মতে সমাজের বনিয়াদটাকেই সংকটাপন্ন করে তোলে, সেই মতবাদকেই আজকের ক্ষয়িষ্ণু সমাজ অমন মরিয়ার মতো আঁকড়ে ধরছে কেন? ফ্রয়েডবাদ নিয়ে এই সাম্প্রতিক উৎসাহটুকু থেকেই প্রমাণ হয় প্রতিবন্ধ-সংক্রান্ত ফ্রয়েডীয় মতবাদটার গোড়ায় গলদ রয়েছে। তার মানে সাইকোএ্যানালিসিসের বিরুদ্ধে অতীত আপত্তিটার ফ্রয়েড যে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন সেই ব্যাখ্যার বৈজ্ঞানিক মর্যাদা নেই। মানুষের সনাতন আত্মাভিমান আহত হবার কথা, কিংবা সভ্যতার বনিয়াদ সংকটাপন্ন হবার কথা—কানে শুনতে যতই রোমাঞ্চকর লাগুক না কেন, এগুলো তাঁর প্রখর কল্পনাশক্তিরই পরিচয়, বৈজ্ঞানিক উপসংহার নয়।
তার মানে কি এই যে সমাজের তরফ থেকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিরুদ্ধে বাধা ওঠবার কথাটাই কল্পনা? সামাজিক প্রতিবন্ধ বলে ব্যাপারটাই কি মিথ্যে? নিশ্চয়ই নয়, যদিও সমাজ বলতে একটা সনাতন ও অন্তর্দ্বন্দ্বহীন কিছু বুঝতে গেলে এই সামাজিক প্রতিবন্ধের কথাটা আগাগোড়াই কাল্পনিক হয়ে দাঁড়ায়। কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, ডারউইন, মার্কস্—এঁদের সবাইকার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিরুদ্ধেই সামাজিকভাবে তীব্র ও তুমুল আপত্তি উঠেছে। বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিরুদ্ধে সামাজিকভাবে মাঝে মাঝে দারুণ বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে বই কি। কিন্তু এই বিক্ষোভের উৎসটা ঠিক কোথায়? পুরো সমাজটা? নিশ্চয়ই নয়। মানুষের সনাতন আত্মাভিমান? তাও নয়। তাহলে?
আসলে মার্কপন্থী বিচার করে দেখান, কোনো একটা বিশেষ সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখবার ব্যাপারে যে-শ্রেণীর স্বার্থ সেই শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে কোনো বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার বা দার্শনিক মতবাদ যখন সংঘাত সৃষ্টি করে, তখনই কায়েমী স্বার্থের খাতিরে ওই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বা দার্শনিক মতবাদের বিরুদ্ধে সমাজে তীব্র সোরগোল সৃষ্টি হয়। এই কথার মূল তাৎপর্যগুলি একে একে দেখা যাক। প্রথমত, সমাজ-ব্যবস্থা বলে ব্যাপারটা সনাতন বা শাশ্বত কিছু নয়। যুগে যুগে মানব-সমাজে মৌলিক পরিবর্তন দেখা দেয়। দ্বিতীয়ত, পুরো সমাজটাকে অন্তর্দ্বন্দুহীন সমজাতীয় কোনো কিছু বলে কল্পনা করা চলে না। সভ্য সমাজ শুরু হবার মুখোমুখি সময় থেকে ধনতন্ত্রের চূড়ান্ত বিকাশ পর্যন্ত সমস্ত সমাজ ব্যবস্থার মুলেই অন্তর্দ্বন্দু। সেই অন্তর্দ্বন্দ্বের নাম শ্রেণীসংগ্রাম—শোষক আর শোষিতের মধ্যে সংগ্রাম, শাসক আর শাসিতের মধ্যে সংগ্রাম। তৃতীয়ত, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও দার্শনিক মতবাদ বলে ব্যাপারগুলি বিশুদ্ধ, নির্লিপ্ত ও নৈর্ব্যক্তিক কিছু নয়, শ্রেণীসংগ্রামের সঙ্গে এগুলির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। অর্থাৎ কোনো আবিষ্কার বা মতবাদ একটা বিশেষ সমাজের শোষক-শাসক শ্রেণীর স্বপক্ষেও যেতে পারে আবার বিপক্ষেও যেতে পারে। আর চতুর্থত, যে-মতবাদ বা যে-আবিষ্কার সামাজিকভাবে যে-শ্রেণীর স্বার্থে আসে সেই শ্রেণী ওই মতবাদকে সমর্থন করে, যে-শ্রেণীর বিরুদ্ধে যায় সেই শ্রেণী এর বিরুদ্ধে বাধা সৃষ্টি করে।
তাঁর নিজের তরফের দৃষ্টান্ত হিসাবে ফ্রয়েড উল্লেখ করেছেন, কোপার্নিকাস আর ডারউইনের কথা। চমৎকার দৃষ্টান্ত, সন্দেহ নেই। কিন্তু কথা হলো, দৃষ্টান্ত দুটির তাৎপর্য কি সত্যিই তাঁর মতবাদের তরফে যায়? নমুনা দুটিকে বিশ্লেষণ করা যাক। কোপার্নিকাসের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি। কিন্তু কোন্ সমাজের, কোন্ শ্রেণীর তরফ থেকে আপত্তি? কেন আপত্তি? য়ুরোপের সামন্ত যুগটার শেষাশেষি যে-অবস্থা তার পটভূমি মনে না রাখলে এ-আপত্তির তাৎপর্য বোঝা সম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে, তখনকার দিনে জমিদার আর পাদ্রী শ্রেণীর কথা। তারাই শোষক, তারাই শাসক আর তাদের শাসনের একটা খুব মোক্ষম অস্ত্র হলো ধর্মমোহ। সেই ধর্মমোহের বিরুদ্ধে তীব্র আঘাত হানলো কোপার্নিকাসের আবিষ্কার। সামন্তযুগের শোষকশ্রেণী খাপ্পা হয়ে উঠবে না কেন? কিন্তু সমাজ বদলালো, শেষ হলো জমিদার-পাদ্রীদের শোষণ-শাসন আর সেই সঙ্গে শেষ হলো কোপার্নিকাসের বিরুদ্ধে ওই তীব্র বিদ্বেষ-প্রচার। কেননা, নতুন যে-শ্রেণী প্রভুর আসনে বসলো তার স্বার্থের সঙ্গে কোপার্নিকাসের ওই আবিষ্কারের অমন সংঘর্ষ নেই। তাই নেই বিদ্বেষ প্রচারের অমন উৎসাহ। মানবাত্মার সনাতন অভিমান যদি ক্ষুণ্ণ করে থাকে, তাহলে আজকের দিনে কোপার্নিকাসের আবিষ্কার আমার আপনার সহজ বুদ্ধিতে পরিণত হলো কী করে? আমাদের এই পৃথিবী যে সত্যিই সৌরজগতের কেন্দ্র নয় সূর্যের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে—এ কথায় আমাদের ইজ্জত খোয়া যাবার কোনো সম্ভাবনা কল্পনা করাই আমাদের পক্ষে আজ রীতিমত কঠিন। কিন্তু তখনকার দিনের ধর্মমোহের সঙ্গে এ-কথার যে কী দারুণ সংঘর্ষ তা সামান্যমাত্র ঐতিহাসিক চেতনার বলে আমাদের পক্ষে আন্দাজ করা একটুও কঠিন নয়। ডারউইনের বেলাতেও একই কথা। কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে তাঁর আবিষ্কারের যতখানি বিরোধ, কায়েমী স্বার্থে সামাজিকভাবে তাঁর আবিষ্কারের বিরুদ্ধে ঠিক ততখানিই কুৎসা-প্রচার করেছে। ডারউইনের বিরুদ্ধেও সবচেয়ে প্রবল আপত্তি রক্ষণশীল শ্রেণীর তরফ থেকে, কেননা ডারউইনের আবিষ্কার এই রক্ষণশীল স্বার্থে আঘাত হেনেছে। সৃষ্টিতত্ত্বের সনাতন এক উপাখ্যানের সঙ্গে রক্ষণশীল শ্রেণীর স্বার্থ প্রকটভাবে সংযুক্ত। তাছাড়া ডারউইনের ব্যাপারে আরও একটা কথা বিশেষ করে লক্ষ্য করা দরকার। তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে মিশেল হয়ে রয়েছে পুঁজিবাদী নীতিকথার বিজ্ঞানম্মন্য নির্লজ্জ প্রচারক ম্যালথাসের মতবাদ—তথাকথিত জানের খাতিরে আত্মীয়বোধের নীতি। এবং পুঁজিবাদী সভ্যতার পরমায়ু যতই ফুরিয়ে আসছে ততোই পুঁজিবাদী দুনিয়ায় ডারউইনের আসল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারটুকুর উপর থেকে ঝোঁক সরিয়ে (কেননা এ-আবিষ্কার শেষ পর্যন্ত পুঁজিপতিদের কায়েমী স্বার্থকেও সম্মান করতে পারে না।) ওই অবৈজ্ঞানিক কল্পনার উপরই ঝোঁক দেবার চেষ্টা। ডারউইনের আবিষ্কার সম্বন্ধে এবং আধুনিক সমাজে ডারউইনের সমালোচনা সম্বন্ধে গ্রন্থান্তরে থেকে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছি। (১৯) আপাতত, স্থান-সংক্ষেপের খাতিরে তার সবটুকু উল্লেখ করা গেল না।
ফ্রয়েড নিজের সঙ্গে ডারউইন আর কোপার্নিকাসের তুলনা করছেন। এই তুলনার মধ্যে বাহুল্য থাকলেও এর ভিত্তিতে যে একেবারে কিছুই নেই তা মনে করাও ঠিক হবে না। তার মানে নিশ্চয়ই এই নয় যে, ফ্রয়েডের মতবাদও বিজ্ঞানের ইতিহাসে কোপার্নিকাস্ আর ডারউইনের মতোই যুগান্তর এনেছে। তার মানে এও নয় যে———ফ্রয়েড নিজে যে-রকম কল্পনা করেছেন—তাঁর মতবাদও মানবাত্মার সনাতন আত্মাভিমানকে সমতুল্যভাবে আহত করেছে বলেই সমজাতীয় প্রতিবন্ধের মুখোমুখি হতে বাধ্য হয়েছে। তার আসল মানেটা এই-ই যে, ফ্রয়েড প্রথম যখন তাঁর মতবাদ পেশ করেছিলেন তখন তাঁর মতবাদও একদিক থেকে কায়েমী স্বার্থের বিরোধিতা করেছিল আর সেই জন্যেই কায়েমী স্বার্থ সামাজিকভাবে ফ্রয়েডীয় মতবাদের বিরুদ্ধে নানান রকম বাধাবিপত্তি সৃষ্টি করেছিল। অবশ্যই কোপার্নিকাস্ আর বিশেষ করে ডারউইন কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে যে আঘাত হেনেছিলেন তা অনেক বেশি গুরুতর, অনেক প্রচণ্ড। তবুও ফ্রয়েডীয় মতবাদও যে একটা সময়ে আপেক্ষিকভাবে কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে গিয়েছিল এই কথাটাও ভোলা ঠিক নয়। তাতে ইতিহাস-বোধ ব্যাহত হবার ভয় এবং ফ্রয়েড যে কেন নিঃসন্দেহেই বুর্জোয়াশ্রেণীর মতবাদগত প্রচারক, সে কথা স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করবার মধ্যেও ফাঁক থেকে যাবার সম্ভাবনা।
মনে রাখতে হবে, সে-সময়ে ফ্রয়েডীয় মতবাদের মূল আওয়াজ ছিল ‘ব্যক্তিগত যৌন-প্রণয়ের’ আওয়াজ, যৌন জীবনে মুক্তির আওয়াজ। এবং এঙ্গেলস্ দেখাচ্ছেন, এই আওয়াজ বুর্জোয়া সভ্যতারই আওয়াজ, বুর্জোয়া সভ্যতার আগে পর্যন্ত এই দাবি তোলবার মতো বাস্তব পরিস্থিতি মানুষের ইতিহাসে দেখা দেয়নি। য়ুরোপীয় সামন্ত যুগেও নয়। যে-যুগে মানুষের যৌন-সম্পর্ককে একেবারে অন্য চোখে দেখবার চেষ্টা। তাছাড়া, যে-সমাজে যে-যুগে ফ্রয়েডের মতবাদ দানা বাঁধছে—সেই সমাজে সেই যুগে, য়ুরোপীয় সামন্ত সভ্যতার সমস্ত চিহ্নই সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি। (১৮৭০-৭৫-এর অস্ট্রিয়া কায়েমী স্বার্থের মধ্যে তখনও সেখানে সামন্ততন্ত্রের স্পষ্ট ভগ্নাবশেষ।) ফ্রয়েডের মতবাদ তাই এই দিক থেকে কায়েমী স্বার্থের বিরোধিতা করেছে আর প্রত্যুত্তরে কায়েমী স্বার্থের কাছ থেকে বিরোধিতাও পেয়েছে। অর্থাৎ, তিনি বুর্জোয়া শ্রেণীর নানান দাবির মধ্যেই একটা দাবি তুলেছিলেন বলেই সেই যুগে বুর্জোয়া বিরোধী রক্ষণশীল শ্রেণী তাঁর বিরুদ্ধে নানান রকম বাধাবিপত্তি সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু সমাজ-সচেতন দৃষ্টিতে সেই বাধাবিপত্তির বিশ্লেষণ না করে, বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন এক “বিশুদ্ধ” মনস্তত্ত্ব দিয়ে এই বাধাবিপত্তির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ফ্রয়েড তাঁর ওই আধা-রহস্যময় ‘প্রতিবন্ধ’-র মতবাদ সৃষ্টি করলেন।
এইখানে একটা কথা খুব স্পষ্টভাবে মনে রাখা দরকার, নইলে প্রগতির ওজুহাত ফ্রয়েডীয় মতবাদ নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত উচ্ছ্বাসের অবকাশ থেকে যাবার সম্ভাবনা। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের তুলনায় ধনতন্ত্রের ওই আওয়াজ—যৌন মুক্তির দাবি, ব্যক্তিগত যৌন প্রণয়ের দাবি—অনেক প্রগতিশীল সন্দেহ নেই। কিন্তু এই প্রগতিটা নেহাতই আপেক্ষিক প্রগতি, কোনো চরম প্রগতি নয়। কেননা, সামন্ততন্ত্রের তুলনায় ধনতন্ত্র স্বর্গ হলেও সমাজতন্ত্রের তুলনায় নরকই। যৌন সম্পর্কের বেলাতেও একই কথা। তাই প্রকৃত প্রগতিপন্থীর পক্ষে, সমাজতন্ত্রীর পক্ষে এই আপেক্ষিক প্রগতিকে চরম প্রগতি মনে করাটা নেহাতই মারাত্মক ভ্রান্তি হবে। মনে রাখা দরকার, মতবাদ এবং প্রয়োগ উভয় দিক থেকেই যৌন মুক্তির এই বুর্জোয়া বা ফ্রয়েডীয় সংস্করণটির মধ্যে ফাঁকি আছে। এঙ্গেলস্-এর মূলসূত্র অনুসরণ করে মতবাদের দিক থেকে যে-ফাঁকি তার আলোচনা একটু পরেই তুলবো। তার আগে প্রয়োগের দিক থেকে ফাঁকির দৃষ্টান্তটা তোলা যাক। জার্মান বৈপ্লবিক আন্দোলনের একটা যুগে তরুণ সমাজতান্ত্রিকদের মনে ফ্রয়েডীয় মতবাদের এই কথাটা একরকম মোহ সৃষ্টি করেছিল, এবং সমাজ-বাস্তবকে পরিবর্তন করবার চেয়ে—যে পরিবর্তন না হলে প্রকৃত যৌন মুক্তির কথা আকাশকুসুমের মতো অলীক হয়েই থাকবে—তাঁরা নিছক এই যৌন মুক্তির আদর্শের উপাসক হতে চাইলেন। ফলে তাঁদের ব্যবহারিক জীবনের প্রকৃত মুক্ত যৌন আদর্শের বদলে জুটেছিলো যৌন অরাজকতার সম্ভাবনা –এ্যানারকিম্। এবং এ-বিষয়ে লেনিনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে তিনি এর অত্যন্ত কঠোর সমালোচনা করেন। যে-ফ্রয়েডবাদের মোহে বৈপ্লবিক কর্মীদের মধ্যে এই এ্যানারকি-এর সম্ভাবনা লেনিনের সমালোচনায় সে-সম্বন্ধে তীব্র, তীক্ষ্ণ মন্তব্য।
আসলে, বুর্জোয়া সভ্যতা বা ধনতন্ত্র মানুষের সামনে যে-সব রঙিন প্রতিজ্ঞা পেশ করেছিল ধনতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে সেগুলির বাস্তব বিফলতা অত্যন্ত করুণ। ব্যক্তিগত যৌন প্ৰণয় বা যৌন মুক্তির আওয়াজ সম্বন্ধে ঠিক এই কথাই। যৌন মুক্তির ওই আওয়াজ বুর্জোয়া বাস্তবে অবারিত গণিকা-প্রথার গ্লানিতে পর্যবসিত। এঙ্গেলস্ দেখাচ্ছেন, এর আসল কারণ হলো প্রকৃত যৌন মুক্তির জন্যে যে সামাজিক প্রস্তুতি প্রয়োজন বুর্জোয়া সভ্যতার কাঠামোর মধ্যে তা বাস্তবে পরিণত হওয়া সম্ভব নয়। সামাজিক প্রস্তুতিটা হলো, মেয়েদের মধ্যে সামাজিক মেহনতের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা, সামাজিক মেহনতের ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের সাম্য কায়েম করা। সামন্ততন্ত্রের আওতায় এ-কথা সম্ভাবনা হিসেবেও বাস্তব ছিল না, ধনতন্ত্রের আওতাতেই প্রথম সম্ভাবনা হিসেবে বাস্তব হলো। কিন্তু এই সম্ভাবনাকে সত্যিই বাস্তবে পরিণত করতে গেলে ধনতন্ত্রের ভিত্তিই কেঁপে ওঠে—ধনতন্ত্রের পক্ষে আর টেকাই সম্ভব হয় না। তাই যৌন মুক্তির যে আদর্শ বুর্জোয়া সমাজে প্রথম শোনা গেলো বুর্জোয়া বাস্তবে সেই আদর্শের চরম অবমাননা।
এই হলো এঙ্গেলস্-এর বিশ্লেষণ: যৌন মুক্তির আদর্শ পুঁজিবাদী সভ্যতারই আদর্শ অথচ এই আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করবার যে অনিবার্য শর্ত—স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সামাজিক মেহনতের সাম্য কায়েম করা—তা ওই বুর্জোয়া সমাজের কাঠামোকেই চৌচির করে দিতে চায়। তাই বুর্জোয়া বাস্তবে বুর্জোয়া আদর্শের অমন করুন পরাজয়।
কিন্তু ফ্রয়েড প্রসঙ্গে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে না। কেননা ফ্রয়েডীয় মতবাদ যে বুর্জোয়া স্বার্থের সঙ্গে যে কী রকম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত তার পক্ষে খুবই জরুরী আরও একটা কথা উল্লেখ করা দরকার। ফ্রয়েড শুধুই যৌন মুক্তির আওয়াজ তোলেননি, বুর্জোয়া স্বার্থের সঙ্গে সমান তাল রেখে আপাত-বৈজ্ঞানিক মনস্তত্ত্বের দোহাই দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, মেয়েরা সত্যিই ছোটো, পুরুষের সঙ্গে সমান সমান হতেই পারে না। মেয়েরা যে ছোটোই তা প্রমাণ করবার আশায় ফ্রয়েড শুধু এইটুকুই বলছেন না যে পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের মধ্যে sublimation বা উৎগতির শক্তি অনেক কম। নারীচরিত্রের একটি সার্বভৌম লক্ষণ হিসেবে তিনি তাঁর বিখ্যাত penis-envy বা ‘লিঙ্গ-ঈর্ষা’-র মতবাদ পেশ করেছেন। এই মতবাদের মূল কথা হলো, পুরুষ-জনন অঙ্গের অনুরূপ একটি অঙ্গ আপন দেহে নেই বলেই সমস্ত মেয়ে মনে-প্রাণে নিজেকে পুরুষের তুলনায় হীন ও হেয় জ্ঞান করে এবং যদিই বা কোনো মেয়ে রোখ করে পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিতে যায় তাহলে বুঝতে হবে তার এই ব্যবহারটা আসলে ওই হেয়-বোধের গ্লানি থেকে আত্মরক্ষার প্রয়াসমাত্র ( defense reaction)। সাধারণ পাঠকের সহজ বুদ্ধির কাছে এই মতবাদটা যতই আষাঢ়ে কথা হোক না কেন, আধুনিক সাইকোএ্যানালিটিক্যাল সাহিত্যের সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনিই জানেন এই মতবাদ নিয়ে কতোই না গুরুগম্ভীর আলোচনা। আপাতত, সে-আলোচনার খুঁটিনাটি উল্লেখ করবার অবসর নেই, কিন্তু সমাজ-সচেতন ব্যক্তিমাত্রই অবাক হয়ে স্বীকার করবেন পুরুষ-প্রধান সমাজব্যবস্থার সমর্থনে এমন অভিনব ও ধূর্ত যুক্তি আর কখনো পেশ করা হয়েছে কিনা তা অত্যন্ত সন্দেহের কথা।
বুর্জোয়া সমাজের দুটো দিকের কথাই ভেবে দেখুন: সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে যৌন মুক্তির আওয়াজ, আবার সমাজতান্ত্রিক আওয়াজের বিরুদ্ধে মেয়েদের হেয় ও হীন প্রতিপন্ন করবার উৎসাহ। এই দুটো কথা স্পষ্টভাবে মনে রাখলে সিগমুণ্ড ফ্রয়েডকে পুঁজিবাদী সভ্যতার অভ্রান্ত প্রচারক বলে শনাক্ত করতে অসুবিধে হবে না। এবং ‘প্রতিবন্ধ’ নাম দিয়ে তিনি যে মতবাদটি পেশ করেছেন তার আসল তাৎপর্যটুকুও এই দিক থেকেই বুঝতে পারা যাবে: পুঁজিবাদী সভ্যতার অভ্রান্ত প্রচারক বলে সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ এককালে তাঁর বিরুদ্ধে বাধা আপত্তি তুলেছিলো। কোনো রকম নিজ্ঞান রহস্যের কথা বলে ওই ‘প্রতিবন্ধ’র ব্যাখ্যা করবার দরকার নেই। আর তাই যদি করতে চান তাহলে আধুনিক দুনিয়ায় মুমূর্ষু ধনতন্ত্র কেন অমন মরিয়ার মতো ফ্রয়েডবাদ নিয়ে মেতে উঠেছে তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে রকমারী গোঁজামিল চালাতে হবে। আর্নস্ট জোন্স যেমন প্রায় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলেছেন, বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে মানুষের সংস্কার দিনের পর দিন দুর্বল হয়ে আসছে। তার মানে, মানুষ বলে জীব বুঝি বিজ্ঞানের জন্মশত্রু। কথাটা কিন্তু বাজে কথাই। কেননা বিজ্ঞান তো আর মঙ্গলগ্রহ থেকে কোনো রকম বিরুদ্ধ আমদানি নয়, মানুষেরই সৃষ্টি। মানুষ কেন বিজ্ঞানের জন্মশত্রু হবে? তা যদি হতো তাহলে মানুষ হাজার বছর ধরে অমন অক্লান্ত পরিশ্রম আর স্বার্থত্যাগ সহ্য করে বিজ্ঞানকে গড়ে তুললো কেন? বিজ্ঞান তো মানুষের পরম সুহৃৎ, মানুষকে মুক্তির পথ দেখায়। কোনো বিশেষ শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থের বিরোধিতা করলে পরই সেই শ্রেণী বিজ্ঞানের শত্রু হতে পারে, কিন্তু সমস্ত মানুষ সম্বন্ধে এমনতর কোনো কথা বলাটা হলো দুনিয়ার কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে ওকালতি করাই; কেননা আজ বিজ্ঞানের অগ্রগতি কায়েমী স্বার্থকে ধ্বংস করার মুখোমুখি হয়েছে।
ফ্রয়েডের ওই তথাকথিত ‘প্রতিবন্ধ’ সম্বন্ধে মতবাদকে বিচার করতে হলে আরও একটি প্রশ্ন তোলা একান্তই দরকার: আজকের পৃথিবীতে যে-সব দেশে মুমুর্ষু ধনতন্ত্রের পক্ষে বাঁচবার জন্যে সবচেয়ে মরিয়ার মতো প্রচেষ্টা সেইসব দেশগুলিতেই ফ্রয়েডীয় মতবাদ নিয়ে আজ এমন মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহ কেন? ধনতন্ত্রের নাগপাশ থেকে যে-সব দেশ মুক্তি পেয়েছে সেই সব দেশে তো এ-আগ্রহের ছিটেফোঁটাও নেই। কোনো রকম নিজ্ঞান রহস্যের কথা তুলে এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া চলে না। কেননা, জবাবটা আসলে সমাজতত্ত্বের কাছ থেকেই পাওয়া সম্ভব। ফ্রয়েডীয় মতবাদ একান্তভাবেই ধনতান্ত্রিক সভ্যতার স্বার্থে প্রণোদিত, তাই সামন্ততন্ত্রের তরফ থেকে কায়েমী স্বার্থ এর বিরুদ্ধে এককালে যে-রকম আপত্তি তুলেছিল আজকের দিনে মুমুর্ষু ধনতন্ত্র সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তার চেয়েও বেশি আগ্রহে এই মতবাদটির উপরই নির্ভর করতে চায়।
ফ্রয়েডীয় মতবাদের সমর্থনে মুমূর্ষু সমাজটার ‘প্রতিবন্ধ’র বদলে মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহই। অবশ্য মনে রাখতে হবে, ফ্রয়েডীয় মতবাদের তরফ থেকে এই উৎসাহ প্রাপ্তির প্রত্যুত্তরে একরকম কৃতজ্ঞতাও দিনের পরদিন প্রকট হয়েছে। কৃতজ্ঞতার এই বিকাশটা বিশেষ করে লক্ষ্য করবার মতো। কেননা, ফ্রয়েডীয় মতবাদ এই ক্ষয়িষ্ণু সমাজটরা কাছ থেকে যত বেশি উৎসাহ পেয়ে চলেছে ততই দিনের পর দিন যৌন মুক্তির ওই পুরনো আওয়াজটা বদলে ফ্রয়েডবাদ এমন সব নতুন ধরনের আওয়াজ তুলছে, যাতে এই মুমূর্ষু সভ্যতার অনেক প্রত্যক্ষ, অনেক নগদ লাভ। অর্থাৎ, ফ্রয়েডীয় শ্লোগানগুলিরও ইতিহাস আছে। প্রথমে ছিল যৌন মুক্তির শ্লোগান। কিন্তু সে সময়ে এই শ্লোগান বুর্জোয়া সভ্যতার পক্ষে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে যতই সুবিধে সৃষ্টি করুক না কেন কিছুদিন পরেই দেখা গেল এই শ্লোগানের উপরই খুবই বেশি জোর দিতে গেলে বুর্জোয়া সভ্যতার পক্ষে চিড় খেয়ে চুরমার হয়ে যাবার ভয়। ফ্রয়েডীয় মতবাদের শ্লোগান তাই বদলালো। Sense of guilt বা ‘পাপবোধে’র উপর ঝোঁক, আর তারপর Aggression বা জিঘাংসার উপর ঝোঁক। এই ‘পাপবোধ’ এবং ‘জিঘাংসাবৃত্তির’ কথা প্রচার করলে মুমূর্ষু ধনতান্ত্রিক সভ্যতার লাভটা কী বিলক্ষণ তা আন্দাজ করা কঠিন নয়। পাপবোধের কথায় সংগ্রামী মানুষের দীপ্ত চেতনা ঝিমিয়ে আসবে, জিঘাংসাবৃত্তির কথা বলে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ সমর্থন করা চলবে। কিন্তু তারপর আরও আছে। Death—instinct বা মরণ-বৃত্তির কথাও। মানুষ যে শুধুই খুন করতে চায় তাই নয়, মরতেও চায়। ফ্রয়েডের কল্পনাশক্তি বাস্তবিকই দুর্ধর্ষ : এই মরণবৃত্তির কথাটা ব্যাখ্যা করে তিনি বলছেন, এ যেন পক্ষভূতের পিছটান। শেষ পর্যন্ত পঞ্চভূত থেকেই তো উৎপত্তি, আমাদের মনের কোণায় এই পঞ্চভূতের দিকে ফিরে যাবার একটা আকর্ষণ থাকা আর বিচিত্র কী? জন্মাদস্য যতঃ। অথচ, এই মরণবৃত্তির মহিমা শুনিয়ে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে কামানের খোরাক জোগাড় করাও কত সহজ!
তার মানে, ওই তথাকথিত প্রতিবন্ধর বদলে ফ্রয়েডীয় মতবাদের কপালে যতই রাজসম্মান জুটেছে ফ্ৰয়েডবাদও ততই পুরনো কালের আওয়াজ ভুলে এখন নতুন নতুন আওয়াজ তুলতে শুরু করেছে, যার দরুন এই মুমূর্ষু সমাজটার প্রত্যক্ষ থেকে প্রত্যক্ষতর নগদ বিদায়। ফ্রয়েডবাদের কথা আর ধনতান্ত্রিক সভ্যতার কথা তাই আলাদা করে দেখা চলে না।
এই তো ‘ফ্রয়েডের ‘প্রতিবন্ধ-সমাচার। এবং ফ্রয়েডের নিজের মতোই সামাজিকভাবে ফ্রয়েডীয় মতবাদের বিরুদ্ধে যে ‘প্রতিবন্ধ’ তা আসলে চিকিৎসা প্রসঙ্গে দেখতে পাওয়া ‘প্রতিবন্ধর ই পরিবর্ধিত সংস্করণ। এই পরিবর্ধিত সংস্করণটিকে যাচাই করবার সুবিধেই বেশি—শুধুমাত্র বৃহত্তর বলেই নয়, বন্ধ ঘরের গোপন কথা তুলে যে রহস্যসৃষ্টির সুযোগ এখানে তা সম্ভব নয়। এবং এই বৃহত্তর সংস্করণটির সম্যক বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যায় এর পিছনে কোনো নির্জ্জান রহস্যের সন্ধান করার পথটা ভুল পথ, কেননা এর পিছনে যেটুকু যাথার্থ্য তা নিছক একটি সামাজিক যাথার্থ্যই।