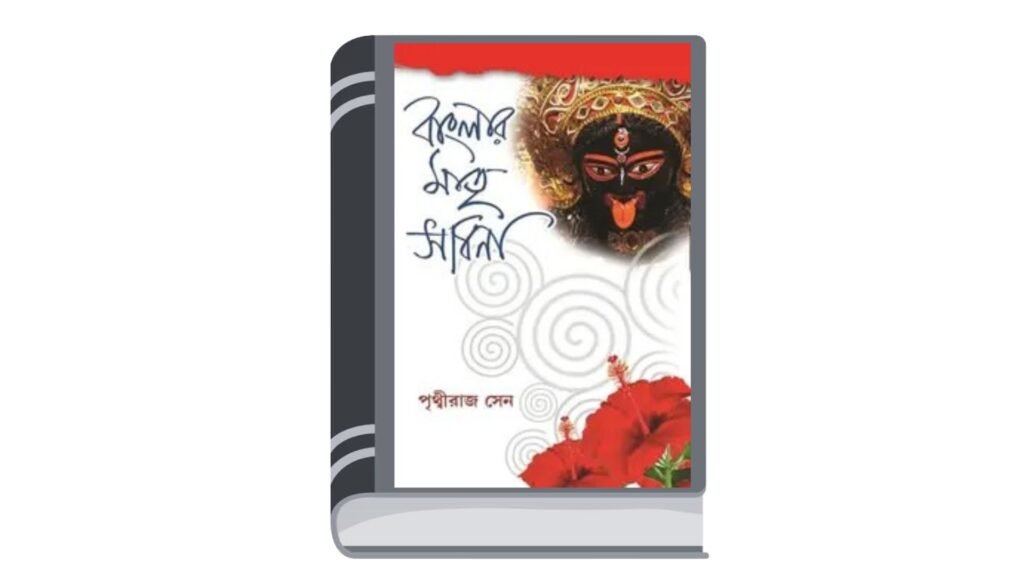অবতরণিকা
দীর্ঘদিন ধরে অবিভক্ত বঙ্গদেশ এবং সন্নিহিত অঞ্চলে শাক্তসাধনার একটি পরম্পরা গড়ে উঠেছে। শাক্ত সাধকেরা জীবনব্যাপী সাধনার মাধ্যমে মহামায়ার উৎস সন্ধানে আত্মনিমগ্ন থেকেছেন। এর পাশাপাশি তাঁরা অসাধারণ সৃজনশীল ক্ষমতার সাহায্যে এমন কিছু শাক্তপদাবলী রচনা করেছেন যার প্রভাব আজও অস্বীকার করা যায় না। বিশ্ব প্রেক্ষপটে নানা ধরনের ঘটনা ঘটে চলেছে। এইসব ঘটনার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাবে মানবমন নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভূতপূর্ব উন্নতিতে মানুষ আগের থেকে আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে শাক্তসাধনা আজ একটি নতুন সন্ধিক্ষণের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।
এ যুগের শাক্ত সাধকেরা স্বীয় স্বীয় প্রতিভার বিচ্ছুরণে আলোকিত করছেন সারা জগৎ। তাঁদের শাক্তসাধনার মধ্যে একদিকে যেমন আধ্যাত্মিক মাত্রা আছে, অন্যদিকে আছে বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধান। এই দুইয়ের সম্মিলনে তাঁদের শাক্তসাধনা আরও বেশি গ্রহণযোগ্য এবং জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।
এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় বাংলার মাতৃসাধনার ওপর আলোকপাত। এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ে প্রবেশ করার আগে আমি মাতৃ ধারণার উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশ সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা করব। একথা ভাবলে অবাক হতে হয় যে, হিন্দু অধ্যাত্ম জগতে মাতৃদেবীর প্রবেশ অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে। এর কারণ কি? মাতৃগর্ভেই তো আমরা দশ মাস দশ দিন অতিবাহিত করি। আমাদের জীবনযাত্রায় পিতার থেকে মাতার অবদান অনেক বেশি। তাহলে? এখানেও কি সেই লিঙ্গজনিত কারণ ক্রিয়াশীল ছিল?
যেহেতু পৃথিবী পুরুষশাসিত, তাই বোধহয় আমরা মাতৃশক্তিকে সেইভাবে স্বীকৃতি দিতে চাইনি। পরবর্তীকালে বাধ্য হয়ে মাতৃশক্তির আরাধনায় মগ্ন থেকেছি।
সমাজবিজ্ঞানীরা বলে থাকেন প্রাকৃতিক শক্তিসাধনার মধ্যে দিয়েই মানবমনে ধার্মিক অনুসন্ধিৎসা এবং ধার্মিক আনুগত্যের সূত্রপাত হয়। অরণ্যচারী মানুষ ছিল একেবারে অসহায়। মাঝেমধ্যেই তাকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলা করতে হতো। একেবারে খালি হাতে লড়াই করতে গিয়ে সে প্রতি মুহূর্তে পরাস্ত হয়েছে। আর তখনই কোনও এক অদৃশ্য শক্তির কাছে নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। প্রথম দিকে এটি ছিল তাঁর পৌরুষের অপমান, কারণ তখনও পর্যন্ত মানুষ শুধুমাত্র বাহুবলের ওপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করার চেষ্টা করত। তাই চোখের সামনে বন্যা অথবা খরা দেখে সেই মানুষ হতো আশাহত। অসহায় আর্তনাদ ছাড়া আর কোনও আকুতি তার মুখ থেকে নিঃসৃত হতে পারত না। কিভাবে এই বন্যা অথবা খরার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায় সে কথা চিন্তা করে মানুষ বন্যার দেবতা এবং খরার দেবতাকে পুজো দিতে শুরু করে। এর পাশাপাশি আরও অনেক দেবতারও আবির্ভাব ঘটে যায়। তাঁরা সকলেই ছিলেন প্রকৃতির এক একটি শক্তির প্রতীক। যেমন আকাশের দেবতা, জলের দেবতা, বাতাসের দেবতা, ভূমির দেবতা ইত্যাদি।
প্রথমদিকে শুধুমাত্র প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকেই মানুষ শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে পুজো করে এসেছে। পরবর্তীকালে অবশ্য মানুষের অধ্যাত্ম সাধনার পরিব্যাপ্তি ঘটে গেছে। তখন আর সে শুধুমাত্র প্রাকৃতিক শক্তির পুজো করে নিজের অনুসন্ধিৎসা মেটাতে পারেনি। আর তখনই অন্যান্য শক্তির প্রতীক স্বরূপ নতুন নতুন দেবদেবীর আবির্ভাব ঘটে গেছে। তাদের কেউ ছিলেন মানুষের অধ্যাত্মসাধনার প্রতীক সঞ্চাত।
এই কটি কথা মনে রেখে এবার আমরা অনুধ্যান সহকারে দেবতাদের উৎস সম্পর্কে অন্বেষণ করব। যুগে যুগে দেবলোকের অবস্থান এবং দেবতাদের চরিত্র পরিবর্তিত হয়েছে। এর কারণ কি? বুদ্ধিজীবীরা মনে করেন যুগে যুগান্তরে মানুষের অনুসন্ধিৎসু ভাবনার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে গেছে। মানুষ ক্রমশ আরও উন্নত হয়ে উঠেছে। তাই পূর্ববর্তী যুগে যে—সব শক্তিকে দেবতার দ্যোতক বা প্রতিভূসম পুজো করা হতো, পরবর্তীকালে তিনি আর সেই সৌভাগ্যের অধিকারী থাকেত পারেননি। কিন্তু কিছু কিছু দেবতা চিরকালই মানুষের শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং ভালোবাসা অর্জন করেছেন। এর কারণ কি? এর কারণ হিসাবে বলা যায় যে ওইসব দেবতাদের মধ্যে এমন কিছু গুণ ছিল যা তাঁদের সর্বজনস্বীকৃতি দিয়েছে।
ঋকবেদে যে দেবতাদের বাসস্থান ছিল তিনটি জায়গায়—পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং দ্যুস্থান। অগ্নি, সোম, পৃথিবী, অপ এবং সরস্বতী ছিলেন পৃথিবীর প্রধান দেবতা। অন্তরীক্ষের দেবতাদের মধ্যে ছিলেন ইন্দ্র, বজ্র ও রুদ্র। দ্যুস্থানের দেবতাদের মধ্যে ছিলেন সূর্য, সবিতা, ঊষা, বরুণ, রাত্রি, যম এবং বৃহস্পতি।
পরবর্তীকালে বলা হয় যে শিব এবং কুবের কৈলাসে বসবাস করেন। অন্যান্য দেবতারা থাকতেন স্বর্গে। দেবতা ছাড়াও স্বর্গে বিচরণ করতেন গন্ধর্ব, অপ্সরা, যক্ষ, কিন্নর ইত্যাদি।
দেবতা কাকে বলে? নিরুক্তকার যাস্ক বলেছেন—দেব—দা নাদ বা দীপনাদ বা দ্যুস্থানে ভবভীতি বা যিনি গমন করেন তিনি দেবতা, যিনি যুক্ত হন বা দ্যোতিত হন বা যিনি দ্যুস্থানে থাকেন তিনিও দেবতা।’
আবার সোমলতাকেও দেবতা বলা হয়েছে, সরস্বতী নদীও দেবতা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন, মণ্ডপকেও বলা হয়েছে দেবতা।
তার মানে যে সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনা এবং পার্থিব বস্তু আর্যদের জীবনচর্যার অঙ্গ ছিল তাঁরা সকলেই দেবতা আখ্যা পেয়েছেন। রূপকের সাহায্যে তাদের মনুষ্য আকৃতি দেওয়া হয়েছে।
দেবতারা যাই হোন না কেন, প্রথমদিকে তাঁদের অঙ্গের মনুষ্য সুলভ আকৃতি ছিল না। মানুষ পরবর্তীকালে এই আকৃতি এনে তাঁদের অস্তিত্বকে আরও সুসংবদ্ধ করার চেষ্টা করেছে।
ঋকবেদের দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ দেবতা। যদিও ইন্দ্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য খুব একটা গুণান্বিত নয়। তিনি বেশিরভাগ সময়ে অসুরদের আক্রমণের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতেন। শুধু তাই নয়, বিপদে পড়লে অন্য দেবতার কাছে ছুটে যেতেন। যদিও তিনি দেবরাজ, তবু তার অনেক চারিত্রিক শৈথিল্য ছিল। রমণী দেখলে লোভী এবং কামার্ত আচরণ করতেন। অথচ এই ইন্দ্রকে উদ্দেশ করে ২৫০টি সুক্ত নিবেদিত হয়েছিল। ঋক্বেদে মোট সুক্তের সংখ্যা ১০১৭। প্রায় ৪ ভাগের ১ ভাগ শ্লোক তাঁকে নিয়ে কেন লেখা হয়?
অনেকে মনে করেন ইন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত চতুর দেবতা। যুদ্ধবিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী। এই গুণকর্মটি আয়ত্ত করার জন্যই তিনি বোধহয় আর্যদের রক্ষক হতে পেরেছিলেন। তিনি দুটি হরিদবর্ণ অশ্বদ্বারা পরিচালিত স্বর্ণরথে অরোহন করেন। সোমরস হল তাঁর পানীয়।
অগ্নি ছিলেন আর্যদের যজ্ঞের ঋত্বিক, পুরোহিত এবং হোতা। অগ্নি আর্যদের চির নমস্য। যদিও অরণির সাহায্যে তিনি উৎপন্ন তাহলেও মনুষ্যরূপে কল্পিত। ঘৃত এবং কাষ্ঠ তাঁর আহার্য এবং হব্য হলো তাঁর পানীয়।
বরুণ জলের দেবতা। ঋকবেদে মিত্র এবং বরুণ একত্রে মিত্রাবরুণ হিসেবে অভিহিত হয়েছেন। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, মিত্র হলেন আলোকের দেবতা আর বরুণ আবরণকারী দেবতা। এই দুই দেবতার মধ্যে কেন এমন সখ্যের সম্পর্ক? এর কারণ কি?
আর্যরা আকাশকে সমুদ্রের সঙ্গে কল্পনা করে তাঁকে জলমগ্ন মনে করতেন। তাই বোধহয় আকাশ ও সমুদ্রের মিলনের ফলে বরুণের উপস্থিতি কল্পনা করা হয়েছে। বরুণ সূর্যের গমনের পথ বিস্তার করেন। তিনি বৃষ্টি দ্বারা স্বর্গ, অন্তরীক্ষ এবং পৃথিবীকে আর্দ্র করেন।
ঋক্বেদে সূর্যকেও মানুষ হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। তিনি হরিৎবর্ণের সাতটি বেগবান অশ্ববাহিত রথে চলাফেরা করেন। বিশ্বভুবন এবং সমস্ত প্রাণীবর্গ জীবনধারণের জন্য সূর্যের ওপর নির্ভরশীল। সূর্য মানুষ এবং পশুর রোগ নিরাময় করেন।
পুষা রথী শ্রেষ্ঠ। তিনি সূর্যের কিরণময় রথচক্রের পরিচালনা করেন। রাত্রি তাঁর পত্নী এবং ঊষা তাঁর ভগ্নী।
বৃহস্পতি জ্ঞানের দেবতা। স্বীয় জ্ঞানের প্রভাবে তিনি যজ্ঞের মন্ত্র উচ্চারণ করেন। মন্ত্রের প্রভাবে শত্রুদের বশীভূত করতেন পারেন। তিনি ইন্দ্রের অনুরূপ আচরণ করেন। তবে ইন্দ্রের মতো হাতে অস্ত্র তুলে নেননি, তিনি শুধুমাত্র মৌখিক উচ্চারিত মন্ত্রের দ্বারাই এমন অসাধ্য সাধন করতে পারেন।
ঋক্বেদে আরও বেশ কয়েকজন দেবতার উল্লেখ আছে। তাঁদের মধ্যে বিষ্ণু, যম এবং সোমের নাম করা যেতে পারে। বিষ্ণু ঋতুর নিয়ামক দেবতা। ঋকবেদের প্রথম মণ্ডলের ১৫ নম্বর সুক্তে বলা হয়েছে যে বিষ্ণু তিন পদক্ষেপে সমগ্র ভুবনে অবস্থান করেন। অর্থাৎ এই ভুবনের সব কিছু বিষ্ণুর অধীন। এভাবেই বোধহয় বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্বকে মেনে নেওয়া হয়েছে।
যম পিতৃলোকের দেবতা। দুটি কুকুর নিয়ে তিনি পিতৃলোকের দ্বার পাহারা দেন। পরবর্তীকালে এই যমকে মৃত্যুর দেবতা রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর তখন থেকে যম সম্পর্কে আমাদের মনে এক ধরনের ভীতিবিহ্বল শিহরণের জন্ম হয়েছে।
সোম পার্বত্য অঞ্চলের লতা বিশেষ। সোমলতা পাথরে পিষে রস বের করে দুধ বা দধির সঙ্গে সেবন করা হতো। এটি শক্তিদায়ক ছিল। সোম ইন্দ্রের শক্তি বর্ধন করত। দেবতা এবং আর্যদের ক্ষেত্রে এটি ছিল এক প্রিয় পানীয়। ঋক্বেদের নবম মণ্ডলের সবকটি সুক্ত সোমের উদ্দেশে রচিত। এতেই প্রমাণিত হয় একসময় সোমরস আমাদের মধ্যে কী ধরনের জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। পৌরাণিক যুগে এসে দেবতাদের পরিমণ্ডল অনেকখানি পাল্টে যায়। এই যুগে ইন্দ্রকে আর প্রধান দেবতা হিসাবে পূজা করা হয়নি। পৌরাণিক যুগের তিন প্রধান দেবতা হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর বা শিব। ইন্দ্র তখন এই তিন শক্তির অধীন হয়ে গিয়েছিলেন।
পৌরাণিক যুগের তিন প্রধান দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মা হলেন স্রষ্টা, বিষ্ণু রক্ষক আর শিব সংহারকর্তা। সংহারের পর শিব আবার সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন তাই তাঁকে শংকর বলা হয়েছে।
ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু স্বর্গে অবস্থান করেন। শংকর বসবাস করেন মহীতে (ভূমিতে)। তিনি হলেন মহীর ঈশ্বর বা মহেশ্বর। যেহেতু মহেশ্বর হলেন ভারতের অনার্য দেবতাদের মতে আদিতম, তাই তাঁকে দেবাদিদেব মহাদেব বলা হয়। পরবর্তীকালে আর্যীকরণের মাধ্যমে তাঁকে কৈলাসে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এজন্য তিনি হলেন কৈলাসপতি। তিনি অত্যন্ত সংযমী এবং স্থির স্বভাবের দেবতা বলে তাঁকে স্থানু বলা হয়।
হিন্দু দেবতাদের মধ্যে শিবের স্থান সব থেকে আগে, কিন্তু তিনি ছিলেন অবৈদিক দেবতা। শুধু তাই নয়, শিবকে আমরা প্রাক্বৈদিক দেবতাও বলতে পারি। প্রাক্বৈদিক সিন্ধু সভ্যতায় শিবের সঙ্গে আমাদের প্রথম দেখা হয়। যেখানে আমরা মৃগ, হস্তী, ব্যাঘ্র, গণ্ডার, মহিষ বেষ্টিত যোগাসনে উপবেষ্টিত ঊর্ধ্ব লিঙ্গ পশুপতি শিবকে একটি শিলমোহরের উপর মুদ্রিত অবস্থায় দেখি। তাঁর উপাসকদের মধ্যেও অবৈদিক আদিম জাতির অবস্থান যেমন অসুর, রাক্ষস ইত্যাদি।
অসুর—রাক্ষস প্রভৃতিরা ছিল শিব ভক্ত। অসুররাজ বাণ ছিলেন তাঁর পরম ভক্ত। লঙ্কেশ্বর রাক্ষসরাজ রাবণও শিবভক্ত হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন।
প্রাগার্য বা অনার্য দেবতা বলেই শিব কোনও যজ্ঞানুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেতেন না। শতপথ ব্রাহ্মণে লেখা আছে দেবতারা যখন স্বর্গে গিয়েছিলেন তখন তাঁদের সঙ্গে শিব ছিলেন না। দক্ষ এই কারণে তাঁর যজ্ঞে শিবকে আমন্ত্রণ জানাননি। শিব এই যজ্ঞ পণ্ড করে তাঁর পৌরুষ এবং সাহসের সাক্ষ্য রেখেছিলেন। তারপর তিনি আর্যসমাজে স্বীকৃতি অর্জন করেন। মনে হয় অনার্যদের মতো আর্যরাও শিবকে রুদ্রের মতো কল্পনা করেছিল। সংস্কৃতে রুদ্র শব্দের অর্থ হল রক্তবর্ণ এবং দ্রাবিড় ভাষাতে শিব শব্দের অর্থ হল রক্তবর্ণ। বৈদিক রুদ্র যে আর্যদের অর্বাচীন এক দেবতা ছিলেন তা বুঝতে পারা যায়; কারণ সমগ্র ঋক্বেদে তাঁর উদ্দেশে মাত্র তিনটি স্তোত্র রচিত হয়েছিল। বৈদিক অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে রুদ্রের ধারাবাহিক বৈরিতা স্থাপিত হয়, অথচ রুদ্র কখনও অসুরদের সঙ্গে বিরোধিতা করেননি। ঋকবেদে বলা আছে রুদ্র সুবর্ণ নির্মিত অলংকার ধারণ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মহেঞ্জোদারোতে আমরা যে আদি শিবের মূর্তি পেয়েছি সেখানেও আদি শিবকে অলঙ্কারভূষিত অবস্থায় দেখা গেছে। বৈদিক রুদ্র দেবতাই যে মহেঞ্জোদারোর আদি শিব এ ব্যাপারে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।
সিন্ধুসভ্যতা হল কৃষিভিত্তিক সভ্যতা। আমরা জানি বিশ্বের বুকে সভ্যতার জন্ম হয় ভূমিকর্ষণ থেকে। ভূমিকর্ষণের ফলেই মানুষ অরণ্যচারী জীবনযাপন ছেড়ে কোনও একটি জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে বাধ্য হয়েছিল। তাই আমরা বিভিন্ন সাহিত্যে শিবকে এক বৃষদ হিসেবে দেখেছি। শূন্যপুরাণের রামাইত পণ্ডিত থেকে শুরু করে শিবরাজের রামেশ্বর শিবের চাষ করার বর্ণনা দিয়েছেন। শিবের মতো জনপ্রিয় দেবতা সারা বাংলায় আর কেউ নেই। তাই বাংলার সর্বত্র অসংখ্য শিবমন্দির ছড়িয়ে আছে।
শিবের পাশাপাশি বিষ্ণু ও ব্রহ্মাও বিশিষ্ট দেবতা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আর এইভাবে আর্য এবং অনার্য দেবতা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছেন। ব্রহ্মা স্বীকৃতি পেয়েছেন মানবসমাজে, তাঁকে বলা হয়েছে বিশ্বের স্রষ্টা। তাঁকে নিয়ে একটির পর একটি পুরাণ লেখা হয়েছে। বৈদিক সাহিত্যে ব্রহ্মাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। বেদ এবং ব্রাহ্মণের সৃষ্টিকর্তাকে হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি বলা হয়েছে। অনেকে বলে থাকেন ব্রহ্মা হলেন এই প্রজাপতির পরবর্তী রূপ।
পুরাণে লেখা আছে যে ব্রহ্মা ‘সৃষ্টি সুখের উল্লাসে’ প্রথমে নয়টি মানসপুত্র তৈরি করেছিলেন। তাঁরা হলেন যথাক্রমে মরীচি, অত্রি, অঙ্গীরা, পুলস্ত, পুলহ, ভৃগু, দক্ষ এবং নারদ এবং এক কন্যা শতরূপা। পুত্রগণ কেউই সহজন্মী ভগিনী শতরূপার সাথে মিলনক্রিয়ায় মগ্ন হতে রাজি হলেন না। অগত্যা মৎস্যপুরাণ অনুযায়ী ব্রহ্মার হৃদয় থেকে কামদেবের জন্ম হয়। আর কামদেব নিজকন্যা শতরূপায় উপগত হন। এই অনাচারের ফলে মনুর জন্ম হয়েছিল।
আবার অন্য একটি কাহিনি অনুসারে শতরূপা মনুর মাতা নন, সরাসরি স্ত্রী। পুরাণে বলা হয়েছে যে ব্রহ্মা প্রথমে যে ন’জন পুত্র সৃষ্টি করেন তাঁরা ছিলেন অপ্রজাপতি অর্থাৎ সৃষ্টি কর্মে অপারগ। ব্রহ্মা তখন বিরাগবশতঃ নিজেই দুই অংশে বিভক্ত হন—একটি অংশ নারী, অন্য অংশ পুরুষ। নারীর নাম শতরূপা এবং পুরুষের নাম মনু। হিন্দু ভাববাদীরা বিশ্বাস করেন মনু কোনও রমণীর গর্ভজাত নন, তিনি ব্রহ্মার দেহ থেকে উদ্ভুত তাই তাঁর আর এক নাম স্বয়ংভূ মনু। মনুর স্ত্রী শতরূপার ছেলে প্রিয়ব্রত, উত্থানপদ ও কন্যা আকুতি ও প্রসুতি। এঁদের ছেলেমেয়েদের থেকেই পৃথিবীতে মনুষ্যজাতির বিস্তার ঘটেছিল।
আর একটি কাহিনি অনুসারে বলা হয় ব্রহ্মার স্ত্রী সরস্বতী—তাঁদের দুই কন্যা দেবসেনা ও দৈত্যসেনা।
বিষ্ণু ইহজগতের পালনকর্তা এবং বৈদিক দেবতা। বেদে বিষ্ণু এবং শিবকে এক ও অভিন্ন হিসেবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। বেদে আমরা সূর্যকে আদিত্য, বিবস্বান, সবিতা, বিষ্ণু ইত্যাদি নামে স্তুতি করেছি।
ঋগবেদের প্রথম মণ্ডলের পনেরো নম্বর সুক্তে বলা হয়েছে যে বিষ্ণু তিন পদক্ষেপে সমগ্র ভুবনে অবস্থান করেন। এবং তিনি ঋতুনিয়ামক দেবতা। বিষ্ণু ঋতুচক্রের অধিকর্তা। তিনি ঋতুচক্রের পরিবর্তনের মাধ্যমে সমগ্র জীবজগতকে বাঁচিয়ে রাখেন। পুরাণ মতে, প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে ও অদিতির গর্ভে বিষ্ণুর জন্ম হয়। স্ত্রী লক্ষ্মী এবং পুত্র কামদেবকে নিয়ে তাঁর সংসার।
বিষ্ণু যে ব্রহ্মার বংশধর সে কথাও আমাদের পুরাণে লেখা আছে। বিষ্ণুর পিতা হলেন কশ্যপ, কশ্যপের পিতা মরীচি এবং মরীচির পিতা ব্রহ্মা। আবার বিষ্ণুর মাতা অদিতি, অদিতির পিতা দক্ষ, দক্ষ পিতা ব্রহ্মা। তাহলে পিতা—মাতা উভয়ের ঠাকুরদাদা হচ্ছেন ব্রহ্মা।
তা সত্বেও ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুর মধ্যে মাঝে মাঝে তীব্র শত্রুতা দেখা গেছে। সংক্ষেপে এই হল হিন্দু—পুরাণ শাস্ত্রানুযায়ী পুরুষ দেবতাদের পরিচয়। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে কবে থেকে স্ত্রী দেবতাদের জয়যাত্রা শুরু হল। এই সময়সীমা নির্ধারণ করা খুব একটা সহজ নয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সভ্যতাতে আমরা নারীকে দেবতা হিসেবে পুজা করতে দেখেছি। মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা প্রভৃতি নগরে দেবী পূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল। সেখানে মৃন্ময়ী মাতৃকাদেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে। অবশ্য আর্যদের ঋক্বেদে দেবতামণ্ডলীতে মাতৃদেবীকে কোনও স্থান দেওয়া হয়নি।
পরবর্তীকালে যখন অনার্য এবং আর্য সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটে তখন প্রাগার্য দেবীসমূহের অনুপ্রবেশ পরিলক্ষিত হয়। বৈদিক যুগের অন্তিম পর্বে আমরা কালী করাল প্রভৃতি অনার্য দেবীর নাম পাই। তখনও পর্যন্ত তাঁরা কিন্তু তাদের মৌলিক স্বরূপতা বা স্বতন্ত্রতা বজায় রেখে অনুপ্রবেশ করতে পারেননি। আর্যরা যখনই তাঁদের দেবমণ্ডলীতে কোনও নতুন দেবতার আগমন ঘটাতেন তখনই চাতুরির সঙ্গে তাঁর আর্যীকরণ করে নিতেন। ধীরে ধীরে আর্যরা উত্তর ভারত ছেড়ে দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের দিকে অগ্রসর হলেন। সেখানকার আঞ্চলিক সংস্কৃতির প্রভাবে তাঁদের ধার্মিক গোঁড়ামি কমতে লাগল। তখন এইসব অনার্য দেবতারা আর্যদের উপাস্য দেবতা হিসেবে পূজিত হতে লাগলেন। এই মাতৃপূজা প্রাগার্য তন্ত্রধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্মকে প্রভাবান্বিত করল।
মাতৃপূজা কিন্তু প্রাগার্য ধর্মের দ্যোতক। তন্ত্রধর্মের মাধ্যমে এটির হিন্দু ধর্মে অনুপ্রবেশ ঘটে। এই বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে গেলে তন্ত্রশাস্ত্র সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান থাকা দরকার।
তন্ত্রধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে নানা মতবাদ প্রচলিত আছে। হিন্দুরা বলে থাকেন বৈদিক ধর্মের মধ্যেই তন্ত্রসাধনার বীজ লুকিয়েছিল। আবার বৌদ্ধরা দাবী করেন তন্ত্রের মূল ধারণাগুলি ভগবান বুদ্ধের প্রবর্তিত এবং প্রদর্শিত নানা মুদ্রা ও মন্ত্রমণ্ডলের মধ্যে লুকিয়ে আছে। কিন্তু গৌতম বুদ্ধ এই জাতীয় গুহ্য সাধন পদ্ধতির সমর্থক ছিলেন বলে মনে হয় না। পরবর্তীকালে অবশ্য বৌদ্ধধর্ম নানাধরনের তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ দ্বারা প্রভাবান্বিত হতে থাকে।
অনেক গবেষক বলে থাকেন তন্ত্রধর্মের আসল উৎপত্তি লুকিয়ে আছে সূত্র কৃঙ্গ নামে এক প্রাচীন জৈন গ্রন্থের মধ্যে। আমরা সকলেই জানি যে তন্ত্রের আচার অনুষ্ঠান অত্যন্ত গূঢ়। এই প্রাচীন জৈন গ্রন্থ অনুসারে গূঢ় সাধন পদ্ধতি এক সময় শবর, দ্রাবিড়, কলিঙ্গ ও গৌড় দেশবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। পরে বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ হিন্দুরা যখন এই তন্ত্র পদ্ধতিকে আত্তীকরণ করেন তখন তাঁরা এর মধ্যে নানা ধরনের আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া প্রবিষ্ট করেন। এই বিশ্বাসকে তাঁরা দার্শনিক অভিজ্ঞতায় সিঞ্চিত করেন।
শক্তি সঞ্চয়ের প্রতিষ্ঠা থেকেই তান্ত্রিক ধর্মের সূত্রপাত হয়। এই শক্তিকে ভর করে যাতে আমরা ধীরে ধীরে একটির পর একটি মার্গ অতিক্রম করে অবশেষে পরমার্থে পৌঁছাতে পারি, তন্ত্রসাধকরা সেই চেষ্টা করে গেছেন।
তান্ত্রিক ধর্মের প্রচলন হয়েছিল শক্তি সঞ্চয়ের জন্য। তান্ত্রিক সাধকেরা এই শক্তিকে তাঁর শরীরে স্থিরীকৃত করার চেষ্টা করতেন। এই শক্তির মাধ্যমেই একটি মার্গ থেকে অন্য মার্গে উন্নীত হওয়ার পথ অন্বেষণ করা হতো। শেষ পর্যন্ত এই শক্তির ওপর নির্ভর করে পরমার্থে পৌঁছতে হবে—এটিই তন্ত্রসাধকদের স্বপ্ন। প্রারম্ভিক স্তরে তন্ত্রসাধনা ছিল পৌরাণিক ধর্মের একটি শাখা। প্রথম দিকে এই ধর্মমত অবিবাহিতা নারীদের পুজো করার বিধি প্রদান করে। কুমারীতন্ত্রে বলা হয়েছে নটি, কাপালিকা, বেশ্যা, ব্রাহ্মণকন্যা, শুদ্র কন্যা, মালাকার কন্যা, নাপিত—রজক ও গোপালক কন্যা তন্ত্রসাধনায় প্রশস্ত। পরে এই প্রথাকে অনুসরণ করে দেবতাদের বিবাহিতা স্ত্রীদেরও দেবী হিসেবে পূজা করার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। দেবতাদের পত্নীরা শক্তিতন্ত্রের দেবী হিসেবে পূজিতা হতে থাকেন। পুরাণ মতে বলা হয়ে থাকে প্রত্যেক দেবতা যদিও একক সত্তার অধিকারী কিন্তু তাঁর চরিত্রে দুটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। আপাতদৃষ্টিতে এই দুটি বৈশিষ্ট্যকে পরস্পর বিরোধী বলে মনে হয়। একদিকে তিনি শান্ত—সমাহিত—সুভদ্র—সুস্নাত, অন্যদিকে অত্যন্ত কর্মশীল ও সক্রিয়। এই চঞ্চল সক্রিয় প্রকৃতিকে শক্তি বলা হয়। পুরাণে দেবতার এই সক্রিয় শক্তিকেই দেবীরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। প্রথমদিকে এটি কয়েকটি দেবীর আরাধনায় স্বীকৃতি পেয়েছিল। আর এই চঞ্চলা শক্তিকেই তন্ত্রসাধনার মূল ভিত্তি ধরা হয়। পরবর্তীকালে একের পর এক নারী—ব্যক্তিত্ব প্রসারিত হয় এবং এই সাধনা অসংখ্য শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তখনও পর্যন্ত আমরা ব্যাপকভাবে নারীশক্তির সাধনা করতে শুরু করিনি। এরপর শিবের স্ত্রী শক্তিসাধনার মূলাধার হয়ে ওঠেন। তাঁকে সমস্ত পৌরাণিক শক্তির প্রতীক বা দ্যোতক হিসাবে গ্রহণ করা হয়। শিবও দেবতাদের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত হতে থাকেন।
এখানে আর একটি কথা মনে রাখতে হবে, তা হল শিবের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের পরিস্ফুটনে তাঁর স্ত্রীর কেবলমাত্র বিপরীত লিঙ্গভুক্তা নন, শিবের গুণাবলীকে তীব্রতর করার জন্যই তাঁকে কল্পনা করা হয়েছে।
স্ত্রী দেবতাদের মধ্যে প্রথমেই আমরা দেবীকে দেখতে পাই। এই দেবী সম্পর্কে বরাহপুরাণ বলছে—ব্রহ্মা কৈলাস পর্বতে শিবদর্শন করতে গেলে শিব বললেন, ‘হে ব্রহ্মা, শীঘ্র করে বলো, কেন তুমি আমার নিকটে এসেছো?’ ব্রহ্মা উত্তরে বললেন, ‘অন্ধক নামে এক পরম পরাক্রান্ত অসুরের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সমস্ত দেবতারা এসেছেন আমার কাছে আশ্রয়ের জন্য। আমি তাঁদের সেই অভিযোগ তোমাকে জানাতে এসেছি।’
ব্রহ্মা তারপর শিবের দিকে তাকালেন। শিব মনে মনে বিষ্ণুকে আবাহন করলেন। এই তিন দেবতা যখনই একত্রিত হলেন তখন তাঁদের তেজোময় দৃষ্টি থেকে পরম লাবণ্যময়ী এক কুমারী কন্যার জন্ম হল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের সামনে তিনি একই অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হল—’আপনি কে? আপনি কেন কালো সাদা এবং লাল রঙের দ্বারা নিজেকে চিহ্নিত করেছেন?’
কুমারী কন্যা রহস্যের ছলে বললেন—’আপনাদের দৃষ্টিপাত থেকেই আমাদের জন্ম। আপনারা কি আপনাদের সর্বব্যাপী শক্তির কথা জানেন না?’
ব্রহ্মা তখন এই নবজাতিকাকে প্রশংসা করে বললেন, ‘তোমার নাম হবে ত্রিকালজয়ী—অর্থাৎ তুমি অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে জয় করতে পারবে। তুমিই হবে বিশ্ববিধাত্রী এবং সকলের রক্ষাকর্ত্রী। তুমি অসংখ্য নামে উপাসিতা হবে। কিন্তু হে দেবী, তুমি যে তিনটি রঙের দ্বারা স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছো, সেই তিনটি রঙ অনুসারে তুমি নিজেকে তিন অংশে বিভক্ত করো।’
দেবী তখন ব্রহ্মার অনুরোধে নিজেকে তিন অংশে বিভক্ত করলেন। একটি সাদা, একটি লাল এবং অপরটি কালো। সাদা অংশটি হলেন লাবণ্যময়ী, আহ্লাদিত কায়া সরস্বতী। ইনি সৃষ্টির কাছে ব্রহ্মার সহযোগিনী রূপে বিরাজ করছেন। লাল অংশটি বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী যিনি বিষ্ণুর সাথে বিশ্বজগৎ রক্ষা করছেন। কালো অংশটি পাবর্তী, যিনি হলেন বহু গুণান্বিতা শিবশক্তিসম্পন্না।
এইভাবে এক নারীশক্তির মধ্যে তিনটি বিশিষ্ট আধার প্রকাশ পেলো। আবার পুরাণ অনুসারে গৌরী হল পার্বতীর আর এক নাম। পার্বতীকে কেন গৌরী বলা হয়? শিব এবং পার্বতী যখন কৈলাসে বসবাস করতেন তখন মাঝে মধ্যে তাঁদের মধ্যে মনান্তর দেখা দিত। একদিন শিব কালো বর্ণের জন্য পার্বতীকে ভর্ৎসনা করেছিলেন। এই ভর্ৎসনায় পার্বতী খুবই ব্যথিত হন। তিনি বেশ কিছুদিনের জন্য শিবকে ত্যাগ করে বনে চলে গেলেন। সেখানে কঠোর তপস্যা শুরু করলেন। তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা তাঁকে বর দিয়েছিলেন যে তাঁর গায়ের রঙ হবে স্বর্ণাভ।
আবার দুর্গা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মার্কণ্ডেয় পুরাণ বলছে—একসময় দৈত্যরাজ মহিষ দেবতাদের যুদ্ধে পরাজিত করেন। দেবতারা তখন সর্বস্ব হারিয়ে এখানে—ওখানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। ইন্দ্র তাঁদের নিয়ে গেলেন ব্রহ্মার কাছে। ব্রহ্মা সকলকে নিয়ে শিবের স্মরণাপন্ন হলেন। অবশেষে ইন্দ্র গেলেন বিষ্ণুর কাছে। দেবতাদের এই শোচনীয় অবস্থা দেখে খুবই ব্যথা পেয়েছিলেন বিষ্ণু। তাঁর মুখমণ্ডল থেকে এক জ্যোতির্পুঞ্জ নির্গত হয়। এই জ্যোতির্পুঞ্জ থেকে মহামায়া নামে এক নারীর জন্ম হল। অন্য দেবতাদের মুখমণ্ডল থেকেও জ্যোতির্প্রবাহ নির্গত হয়েছিল। এইসব জ্যোতিই মহামায়ার ভেতরে প্রবেশ করে। তখন তিনি বহ্নি পর্বতের মতো আলোকজ্জ্বল মূর্তি ধারণ করেন। দেবতারা এই ভীষণ মূর্তির হাতে তুলে দিলেন তাঁদের অস্ত্র সম্ভার। সঙ্গে সঙ্গে সেই সুসজ্জিতা দেবী চিৎকার করে আকাশে উঠে গেলেন। দৈত্যকে সংহার করে দেবতাদের দুর্গতি দূর করলেন। তখন থেকেই তিনি দুর্গা নামে প্রসিদ্ধা। মার্কণ্ডেয় পুরাণে এই গল্পটি বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে।
সেখানে বলা হয়েছে যে, ত্রেতাযুগের শেষে শুম্ভ—নিশুম্ভ দুই দৈত্য দশ হাজার বছর ধরে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। তাঁদের স্তুতিতে প্রসন্ন হয়ে বাধ্য হয়ে স্বর্গ থেকে শিব নেমে আসেন। এই দুই দৈত্য শিবকে অভিবাদন জানালেন। শিব তাঁদের মনোবাসনার কথা জানতে চাইলেন। দৈত্যদ্বয় অমরত্বের বাসনা জানালেন। শিব অসম্মত হয়ে অন্য বর দিতে চেয়েছিলেন।
দুই দৈত্য আবার কঠোর তপস্যায় মগ্ন হলেন। দেখতে দেখতে আরও এক হাজার বছর কেটে গেলো। তাঁদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে শিব আবার আবির্ভূত হলেন। দুই দৈত্য আবার অমরত্বের প্রার্থনা করলেন। শিব এই বর দিতে অস্বীকার করে চলে গেলেন।
এবার শুম্ভ—নিশুম্ভ আগুনের ওপর মাথা নিচের দিকে রেখে তপস্যা করতে শুরু করলেন। এইভাবে আটশো বছর কেটে গেলো। অবশেষে দুই তপস্বীর গলা দিয়ে রক্ত নির্গত হল। দেবতারা বুঝতে পারলেন এবার এঁরা দু’জন অমরত্বের অধিকারী হবেন। স্বর্গের সিংহাসন ছিনিয়ে নেবেন। সঙ্গে সঙ্গে দেবতারা ইন্দ্রকে নিয়ে একটি জরুরী সভা ডাকলেন। ইন্দ্রের কাছে সকলেই নিজেদের অসহায় অবস্থার কথা নিবেদন করলেন। ইন্দ্রের পরামর্শ অনুযায়ী স্বর্গের সুন্দরী অপ্সরা রম্ভা এবং তিলোত্তমাকে দিয়ে প্রেমের দেবতা কন্দর্পকে পাঠানো হল। তাঁরা সকলে মিলে ওই দুই দৈত্যের ইন্দ্রিয় বাসনা পূর্ণ করবেন।
কন্দর্প ফুলশরে উভয়কে বিদ্ধ করলেন। তখন ধ্যানমগ্নতা থেকে উঠে তাঁরা দেখতে পেলেন দুই রূপসী নারীকে। দুই নারীর মায়াজালে দুই তপস্বী আকৃষ্ট হলেন। রমণীদ্বয়ের সঙ্গে তাঁরা পাঁচ হাজার বছর কাটিয়ে দিলেন। তারপর তাঁদের আত্মোপলব্ধি এলো।
শুম্ভ—নিশুম্ভ বুঝতে পারলেন যে, এমনভাবে লালসা ভরা জীবন কাটানো ঠিক নয়। তাঁরা বুঝতে পারলেন এসবই হল ইন্দ্রের ষড়যন্ত্র। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা অপ্সরীদের স্বর্গে বিতারণ করে আবার তপস্যা শুরু করলেন। শরীর থেকে মাংস কেটে নিয়ে তা দগ্ধ করে শিবকে নৈবেদ্য দিতে থাকলেন। এইভাবে আরও এক হাজার বছর কেটে গেল। ধীরে ধীরে তাঁরা কঙ্কলাসারে পরিণত হলেন।
শিব আবার আবির্ভূত হলেন। এবার শিব বর দিয়ে বললেন, একদিক থেকে তোমরা সম্পদ ও শক্তিতে অন্য দেবতাদের অতিক্রম করতে পারবে। কিন্তু আমি অমরত্ব বর দিতে পারব না।
সম্পদ এবং শক্তিতে বলীয়ান হয়ে দৈত্যরা দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। তুমুল সংঘর্ষের পর শেষ পর্যন্ত তাঁরা এই যুদ্ধে জয়যুক্ত হলেন। দেবতারা আবার সব কিছু হারিয়ে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করলেন। ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু সকলকে শিবের স্মরণাপন্ন হতে বললেন। শিব সব কথা শুনে নিজের নিরুপায় অবস্থার কথা ঘোষণা করলেন। কিন্তু দেবতারা শিবকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে তাঁর আশীর্বাদের কারণে আজ দেবগণ ধ্বংস হচ্ছেন। তখন শিব বললেন সকলে মিলে যেন দুর্গার স্মরণাপন্ন হন। একমাত্র দুর্গাই দেবতাদের এই অবস্থা থেকে বাঁচাতে পারবেন কারণ তিনি অনন্যা শক্তির অধিকারিণী।
দেবতারা তখন কঠোরভাবে দুর্গার তপস্যা শুরু করলেন। কিছুকাল পরে দেবী ভুবনেশ্বরী রূপে আবির্ভূত হলেন। তিনি দেবতাদের অভয় দান করলেন। তারপর এক সাধারণ নারীর বেশে জল—কলসী কাঁখে নিয়ে দেবতাদের মাঝখান দিয়ে চলে গেলেন।
দেবী ভুবনেশ্বরী হিমালয় পর্বতে আরোহণ করলেন। সেখানে চণ্ড এবং মুণ্ড নামে শুম্ভ—নিশুম্ভের দুই দূত বাস করত। এই দুই দৈত্য দেবী পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানোর সময় দেবীর ভুবনমোহিনী রূপ দেখে তাঁদের প্রভুদের কাছে এই খবর পাঠিয়ে দেয়। সব শুনে শুম্ভ সুগ্রীবকে দূত করে দেবীর কাছে পাঠালেন।
সুগ্রীব দেবীকে জানালেন ত্রিজগতের সমস্ত সম্পদ এখন শুম্ভের অধীন। এতদিন পর্যন্ত যে সমস্ত নৈবেদ্য দেবতাদের উদ্দেশে নিবেদন করা হতো, এখন তা শুম্ভকে দেওয়া হয়। দেবী যদি শুম্ভের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেন তাহলে তিনি অতুল ধনৈশ্বর্যের অধিকারিণী হবেন। তার মহিমা বহুগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে।
দেবী বুঝতে পারলেন শুম্ভের এই প্রস্তাবের মধ্যে একটা ষড়যন্ত্র লুকিয়ে আছে। তিনি ছিলেন ধীর স্বভাবের রমণী। তিনি বললেন, ‘এই প্রস্তাব খুবই ভালো। কিন্তু আমি স্থির করেছি যে—পুরুষ আমাকে পরাস্ত করতে পারবেন, আমি তাঁকেই আমার জীবনসঙ্গী হিসাবে নির্বাচিত করব।’
সুগ্রীব এই কথা শুনে খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তবুও তিনি তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ না করে বললেন, ‘হে দেবী, আপনি কি আমার প্রভুকে চেনেন? আমার প্রভুর সামনে ত্রিজগতের কোনও মানব, দানব, দৈত্যরাক্ষস এমনকি দেবতারা পর্যন্ত যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারে না। তাহলে একজন নারী হয়ে কিভাবে আপনি আমার প্রভুর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করছেন? আপনি কি একবার ভেবে দেখবেন, এর ফলে কি মারাত্মক পরিণতি আপনার হতে পারে। যদি আমার প্রভু আদেশ করতেন, তাহলে এতক্ষণ আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতাম না। আমি বলপূর্বক আপনাকে অপহরণ করে নিয়ে চলে যেতাম।’
দেবী আবার তাঁর শান্ত মনের পরিচয় প্রদান করলেন। একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁর সৃষ্টি হয়েছে। এই ব্যাপারটি তিনি জানেন। তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ, কিন্তু এগুলো আমার জন্মজন্মান্তরের সিদ্ধান্ত। আমি কখনই আমার অঙ্গীকার থেকে বিচ্যুত হতে পারব না। আপনি যদি আপনার প্রভু সম্পর্কে এতখানি নিঃসন্দেহ হন, তার শক্তিমত্তার কথা আপনি জানেন, তবে দ্বিধা করছেন কেন? আমার স্থির বিশ্বাস তিনি প্রত্যক্ষ সংগ্রামে আমাকে পরাস্ত করতে পারবেন। তখন তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হবে।’
সুগ্রীব তাঁর প্রভুর কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বললেন। শুম্ভ ভাবতে পারেননি যে এক সাধারণ নারী তাকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করবে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রধান সেনাপতি ধূম্রলোচনকে ডেকে পাঠালেন। হিমালয়ে গিয়ে দেবীকে চুলের মুঠি ধরে নিয়ে আসার আদেশ দিলেন। তারপর বললেন—’যদি কেউ দেবীকে উদ্ধার করার জন্য ছুটে আসেন, তাহলে তুমি সেই পাপাত্মাকে হত্যা করো।’
সেনাপতি ধূম্রলোচন হিমালয়ে পৌঁছে গেলেন। তিনি তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠস্বরে দেবীর কাছে তাঁর প্রভুর ইচ্ছের কথা জানালেন। দেবী মৃদু হেসে বললেন, ‘ঠিক আছে, আপনি যদি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান, আমার আপত্তি নেই।’
অবশেষে ধূম্রলোচন অস্ত্রধারণ করলেন। ওই বীরপুরুষ এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে দেবী এমন গর্জন করলেন যে তিনি ভস্মীভূত হলেন। তাঁর সেনাবাহিনী ধ্বংস হল। পলাতক সৈন্যদের মুখে একথা শুনে শুম্ভ এবং নিশুম্ভ চণ্ড ও মুণ্ডকে পাঠালেন। তাঁরা পাহাড়ের কাছে চলে এলেন। দেখলেন হাস্যময়ী এক নারীকে। এবার আবার এক মহা সংগ্রাম শুরু হলো। ওই দেবী একে একে অনেক রাক্ষসকে বধ করলেন। তারপর মুণ্ডের চুলের মুঠি ধরে তাঁর মাথা কেটে ফেললেন। মুখের ওপর সেই কর্তিত মস্তক রেখে তাঁর রক্ত পান করতে লাগলেন। মুণ্ডকে এই রূপে নিহত হতে দেখে এগিয়ে এলেন চণ্ড।
দেবী তখন সিংহের পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়লেন চণ্ডের ওপর। ঠিক যেভাবে তিনি মুণ্ডকে হত্যা করেছিলেন, সেইভাবে চণ্ডকেও শেষ করলেন। সেনাবাহিনীর অনেককে ধ্বংস করলেন। পান করলেন তাদের শেষ রক্তবিন্দু।
দৈত্যদের কাছে এই ভয়ংকর খবর পৌঁছে গেল। এবার সেখানে দেখা দিল দারুণ বিশৃঙ্খলা। শেষ পর্যন্ত বোঝা গেল এই যুদ্ধে তাঁরা বোধহয় জয়লাভ করতে পারবে না।
চোখের নিমেষে সমস্ত সৈন্যকে নিহত হতে দেখে শুম্ভ—নিশুম্ভের প্রধান সেনাপতি রক্তবীজ সামনে এসে দাঁড়ালেন। দেবী তাঁকেও আঘাতে জর্জরিত করতে থাকলেন। এখনে এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল। মাটিতে পড়ে যাওয়া প্রতিটি রক্তবিন্দু থেকে হাজার হাজার দৈত্যের জন্ম হল। শক্তিসামর্থ্যে যারা রক্তবীজের সমতুল্য। এই শত্রু সৈন্যরা দেবী দুর্গাকে ঘিরে ফেলল। এই দৃশ্য দেখে দেবতারা ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। এমনকি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও ভাবলেন এবার এই যুদ্ধে দেবী বোধহয় পরাস্ত হবেন। হঠাৎ নেমে এলেন চণ্ডী নামে এক দেবতা। তিনি মহামায়াকে সাহায্য করলেন। চণ্ডী, মহাকাল, কালী হিসাবে রক্তবীজসহ শুম্ভ—নিশুম্ভকে নির্মমভাবে সংহার করেছিলেন। আর এইভাবেই বোধহয় তিনি শিবের ভুল সংশোধন করেন।
এই গল্পকাহিনি মার্কণ্ডেয় পুরাণে মহাদেবী বা মহামায়ার অংশ হিসাবে দুর্গার সাথে কালীকে একাত্ম করে দিয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন যুদ্ধে এই দেবী নানা ধরনের সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। যেমন দুর্গা হিসাবে তিনি দৈত্যদের হত্যা করেছেন। তেমনি দশভুজা হিসেবে তিনি দৈত্যদের সেনাবাহিনীর একট অংশকে বধ করেন। মুক্তকেশী হিসেবে অন্য সেনাবাহিনীকে সংহার করেছিলেন। জগদ্ধাত্রীরূপে জগৎকে সব রকমের বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। সিংহবাহিনী রূপে লড়াই করেছেন রক্তবীজের বিরুদ্ধে। কালী রূপে রক্তবীজকে হত্যা করেন। মহিষমর্দিনী হিসাবে মহিষাসুরকে বধ করেন। তারা রূপে শুম্ভকে তার আসল মূর্তিতে নিধন করেন। ছিন্নমস্তা রূপে নিশুম্ভকে হত্যা করেন। জগৎ গৌরী রূপে দেবতাদের কাছ থেকে প্রশস্তি এবং ধন্যবাদ লাভ করেছিলেন।
এখানে আমরা দেবীর বিভিন্ন নামের কথা বললাম। এই নামগুলির মাধ্যমেই তাঁর শক্তির বিভিন্ন রূপরেখা নির্ধারিত হয়েছে। কিন্তু এখানে প্রধান দেবী দু’জন—দুর্গা এবং চণ্ডী। তাঁদের আলাদা আলাদা নাম যেমন— দুর্গা, মহামায়া, ভুবনেশ্বরী, দশভুজা, জগদ্ধাত্রী এবং জগৎগৌরী হিসেবে পরিচিতি। চণ্ডী যেমন কালী, তারা, মুক্তকেশী, ছিন্নমস্তা নামে পরিচিতা।
মার্কণ্ডেয় পুরাণে এসে দুর্গা এবং কালীকে দেবী হিসেবে পাওয়া গেল। যদিও কোনও কোনও শাস্ত্রে লেখা আছে যে এঁরা অভিন্ন, কিন্তু এঁদের সৃষ্টি হয়েছে পৃথক পথে। পার্বতী দক্ষ প্রজাপতির কন্যা ও শিবের স্ত্রী। দুর্গা হলেন বিষ্ণুর ভগিনী এবং শিবের স্ত্রী। দুর্গা বা পার্বতীর সঙ্গে কালীর কি সম্পর্ক তা এখনও অস্পষ্ট। যে চণ্ডীর মাধ্যমে আমরা কালীকে পেলাম সেই চণ্ডীই ছিলেন অজ্ঞাতকুলশীলা। মার্কণ্ডেয় পুরাণে তাঁর কোনও পরিচয় রাখা হয়নি।
চণ্ডীকেই আমরা কালী নামে অভিহিত করেছি বলে মনে হয়। এছাড়া আরও কিছু নাম দেওয়া হয়েছে, যেমন প্রলয়ংকরী, করালী কালী, কৃষ্ণকায়া ইত্যাদি।
হিন্দুধর্মে দেবীসাধনা পৌরাণিক মতবাদের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। কারণ বৈদিক সাধনাতে ছিল শুধু দেবসাধনা। দেবসাধনাই পৌরাণিক যুগে দেবীসাধনায় কিভাবে রূপায়িত হল তা ভেবে দেখার বিষয়। এর আগে আমরা অন্য বিষয়ের ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা করব। প্রতি দেবতার মধ্যে এমন এক শক্তি ছিল যা স্ত্রীরূপে দেবীর মধ্যেও বিরাজমানা। পরবর্তীকালে আমরা কেন দেবী পূজার প্রতি বেশি আসক্ত হলাম? বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানীরা বলে থাকেন মানুষের মন তখন উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। মানুষ সৃষ্টি কর্মে নারীর সাহচর্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছে। তখন থেকে আমরা মাতৃসাধনায় আত্মমগ্ন থাকার চেষ্টা করেছি।
শাক্ত মতে প্রতিটি নারীই ঈশ্বরের প্রকৃতি হিসাবে অবস্থান করে। এই শক্তিসাধনার পদ্ধতিটিকে নানাভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই বিভাগের সংখ্যা দশ। মনে হয় বিষ্ণুর দশটি অবতারের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করার জন্যই দেবীর দশটি মূর্তির কথা বলা হয়েছে।
আবার দেবী হলেন মহাজ্ঞানের উৎস এক মহাবিদ্যার প্রতীকী স্বরূপ। মহাবিদ্যাকে দশটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একেকটির সাথে একেকটি বিদ্যা সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে। এই বিষয়ে যে মন্ত্র আছে সেগুলি বিশ্লেষণ করলে আমরা বুঝতে পারি যে কীভাবে অধ্যাত্ম—সাধকবৃন্দ দেবীশক্তির স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন।
কালী হলেন উলঙ্গ, তিনি সহাস্যবদনা, চতুর্ভুজা, কৃষ্ণবর্ণা এবং দিব্যরূপিণী। তাঁর গলদেশে নরমুণ্ডমালা বিদ্যমান। বাম ভাগে নীচের হাতে আছে অভয়মুদ্রা। অপর হাতে বরমুদ্রা। তিনি শিবরূপ শবের ওপর সদম্ভে দণ্ডায়মানা।
এবার আমরা শক্তির দ্বিতীয় রূপ তারার কথা বলব। তারা ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিতা। লম্বোদরী এবং ভয়ংকরা। তাঁর গলদেশে নরমুণ্ডমালা বিরাজমান। তিনি চতুর্ভুজা, নব যুবতীরূপা। এক শবদেহের ওপর তাঁর বামপদ বিন্যস্ত করেছেন। কাশ্মীরে তাঁকে বিশেষভাবে পূজো করা হয়।
ষোড়শী ষোলো বছর বয়স্কা সুন্দরী কিশোরী, বিশেষ করে মালাবারে তাঁর পুজো হয়ে থাকে।
উদিত সূর্যের মতো দেহকান্তিসম্পন্না হলেন ভুবনেশ্বরী। তাঁর কপালে অর্ধচন্দ্র এবং মস্তকে মুকুট। তিনি পীনোন্নত পয়োধরা সম্পন্না, ত্রিনয়নের অধিকারিণী। চতুর্ভুজা ও সহাস্যবদনা।
ভৈরবী উদয়কালীন সূর্যের মতো দেহকান্তি সম্পন্না। তাঁর কপালে অর্ধচন্দ্র এবং তিনি রক্তবর্ণা। হৌমবস্ত্র পরিহিতা। তাঁর গলায় মুণ্ডমালা। মাথায় মুকুট। তিনি চতুর্ভুজা। তাঁর হাতে জপমালা এবং পুস্তক, অভয়মুদ্রা ও বরমুদ্রা।
এবার আমরা ছিন্নমস্তার কথা বলব। ছিন্নমস্তা ষোড়শবর্ষীয়া কিশোরীর মতো। তাঁর স্তনদ্বয় স্থূল ও উন্নত। তিনি আলুলায়িত কুঞ্চিত কুন্তল সম্পন্না, বিবসনা এবং ভয়ংকরী। এক হাতে রক্তমাখা তরবারি, অন্য হাতে নিজের ছিন্নমস্তকধারিণী। তাঁর সর্বাঙ্গে রক্তের আলপনা।
ধূমাবতী বিবর্ণ এবং বিগত যৌবনা। তাঁকে দেখে মৃত্যুর প্রতীক বলে মনে হয়। তিনি এক বিধবা। কাকধ্বজ রথে আরোহণ করে ধুম্ররূপে বিরাজ করেন।
বগলা অবস্থান করেন সুধাসাগরের মধ্যে মণিমাণিক্য নির্মিত এক সিংহাসনে। তিনি পীতবর্ণা, মাল্যবিভূষিতা। তিনি দ্বিভুজা এবং পীতবর্ণ বস্ত্র পরিহিতা।
মাতঙ্গী শ্যামবর্ণা, অর্ধচন্দ্রধারিণী এবং ত্রিনয়না। রত্ননির্মিত সিংহাসনে উপবিষ্টা। তিনি বিশিষ্ট শ্রেণীর নারী হিসেবে শোভিতা।
অবশেষে আমরা দেবীর র্সবশেষ অবতার দেবী কমলার কথা বলব। কমলার দেহকান্তি তপ্ত কাঞ্চনের মতো। রক্তমুকুটে তাঁর মস্তক বিভূষিতা। তিনি তাঁর করে পঞ্চবস্তু ধারণ করেছেন। পদ্মফুলের উপর উপবিষ্টা। তিনি সকলকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেন।
তান্ত্রিক সাধকেরা তন্ত্র—মন্ত্রের মাধ্যমে এই দশ দেবীর পূজা করে থাকেন। তাঁরা পূজা পদ্ধতির মধ্যে বিভিন্ন নিয়ম আনয়ন করেছেন। আবার মা অষ্টমাতৃকার পূজাও প্রচলিত আছে। এই অষ্টমাতৃকা হলেন—(১) বৈষ্ণবী (২) ব্রাহ্মী বা ব্রাহ্মণী—ইনি ব্রহ্মার চারটি মুখমণ্ডল যুক্তা (৩) কার্তিকেয়ী—তাঁকে মুরুগীও বলা হয়, (৪) ইন্দ্রানী, (৫) যোনি, (৬) বরাহি—তাঁর সাথে বিষ্ণুর বরাহ অবতারের মিল আছে, (৭) দেবী বা ঈশানী, ইনি শিবের পত্নীরূপে বর্ণিত। তাঁর এক হাতে ত্রিশূল এবং (৮) লক্ষ্মী—ঐশ্বর্যের, অধিষ্ঠাত্রীর দেবী।
অষ্টমাতৃকারা হলেন বরপ্রদায়িনী এবং বলদাত্রী দেবী। দেবীর অভিব্যক্তির আর একটি শ্রেণীকে যোগিনী বলা হয়। যোগিনীরা হলেন দুর্গার সহচরী। তাঁরা নানা সময়ে নানাভাবে দুর্গাকে সাহায্য করে থাকেন। যোগিনীরা সংখ্যায় ৬৪ জন। তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন ভৈরবী। তিনি দশমহাবিদ্যার অন্যতমা।
দেবীর অভিব্যক্তির আরও দুটি শাখা আছে—ডাকিনী এবং সাকিনী। তারা দেবীর সর্বক্ষণের সঙ্গিনী কিন্তু বিরক্তিকর স্বভাবের রাক্ষসী। এঁদের মধ্যে আছেন চণ্ডী এবং কালী। এই ডাকিনী, কালী আবার দশমহাবিদ্যার অন্যতমা।
তন্ত্র থেকে কালীমূর্তির যে পরিচয় পাওয়া যায় তা হল এইরকম—তন্ত্রমতে এমন এক কালীকে সুরা ও হোমসহ পূজা করা উচিত যাঁর প্রশস্ত ব্যাদানকৃত ভয়ংকর মুখ এবং আলুলায়িত কেশরাশি। তাঁর চারটি হাত আছে এবং নিজ হাতে হত্যা করা দৈত্যদের মুণ্ডদ্বারা খচিত মুণ্ডমালা ধারণ করেন। তিনি এই দৈত্যদের রক্ত নিজে পান করেন। তিনি কর্ণাঙ্গুরীয় পরিধান করেন। দু—হাতে দুটি মৃতদেহ বহন করেন। তাঁর দাঁতগুলি ভয়ংকর, যার চেহারা বিশ্রী, প্রজ্জ্বলিত চিতার মধ্যে বাস করেন। তিনি তাঁর স্বামী মহাদেবের বক্ষদেশে পা রেখে দণ্ডায়মানা অবস্থায় আছেন।
এই হল পৌরাণিক মতে দেবী প্রতিমার বর্ণনা। আর দেবী প্রতিমার পুজো পদ্ধতি যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। পরবর্তীকালে তন্ত্র সভ্যতার আধিপত্যের সময় তন্ত্রমত অনুসারে এই দেবীদের পুজা করা হয়েছে। এভাবেই ধীরে ধীরে ভারতীয় সংস্কৃতিতে দেবীপুজা আগের থেকে অনেক বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।
এই গ্রন্থে আমরা অবিভক্ত বঙ্গদেশের মাতৃসাধনার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করব। বিদগ্ধ পাঠকমণ্ডলীর কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, তারা যদি এই গ্রন্থটি পড়ে কোনও বিষয়ে তাঁদের অভিমত প্রকাশ করতে চান তাহলে অবিলম্বে প্রকাশকের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তাঁদের যে কোনও ইতিবাচক সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করা হবে।