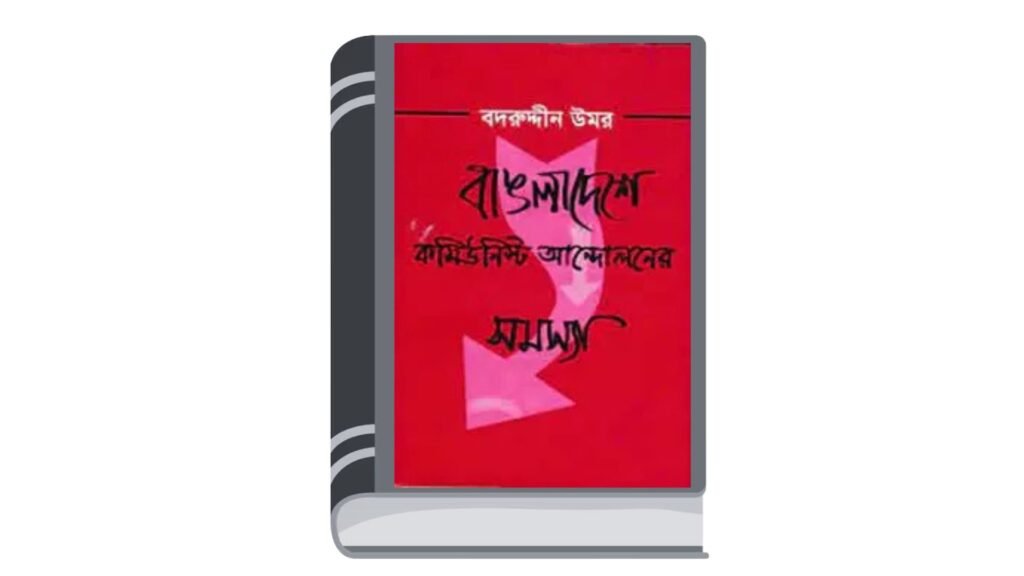বাঙলাদেশে সামন্ত সংস্কৃতি ও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব
১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রাক্কালে তৎকালীন পূর্ব বাঙলায় জনগণের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে সামন্তবাদের প্রভাব যথেষ্ট প্রবল ছিলো। বস্তুতঃপক্ষে সেই প্রভাব ব্যতীত এ অঞ্চলে পাকিস্তানের মতো একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতো না।
ধর্মকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চিন্তা যে সমাজে প্রবল থাকে সে সমাজের অর্থনৈতিক, বিশেষতঃ সাংস্কৃতিক জীবন সামন্তবাদের খুঁটিতেই মোটামুটি বাঁধা থাকে। ঐতিহাসিকভাবে এটা সত্য। আমাদের দেশে ধর্মকেন্দ্রিক রাজনৈতিক চিন্তার অপর নাম সাম্প্রদায়িকতা। এই সাম্প্রদায়িকতার সামগ্রিক চরিত্র মধ্যশ্রেণীর আর্থিক জীবনের রেষারেষির দ্বারা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হলেও সামন্ত অর্থনীতি এবং সামন্ত সংস্কৃতির মধ্যেই তার মূল গভীরভাবে প্রোথিত।
পূর্ব বাঙলা পূর্ব পাকিস্তানে পরিণত হওয়ার পর থেকে এদেশের গ্রামীণ ও কৃষি অর্থনীতির মধ্যে দুই ধরনের পরিবর্তন শুরু হয়। প্রথম পরিবর্তন হচ্ছে, গ্রামাঞ্চলের প্রধান শোষক শ্ৰেণী ভূমি মালিক, মহাজন, ইজারাদার প্রভৃতির সাম্প্রদায়িক চরিত্র পরিবর্তন। ১৯৪৭ সালের অগাষ্ট মাসের পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু জমিদার, জোতদার, মহাজন, ইজারাদার প্রভৃতিরা নিরাপত্তা (সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির জন্য) ও আর্থিক বিকাশের সম্ভাবনার অভাবে (অমুসলমানদের প্রতি পাকিস্তান সরকারের বৈরী মনোভাবের জন্য) উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, শিক্ষক, ব্যবসায়ী প্রভৃতিদের মতই ব্যাপকহারে দেশ ত্যাগ করতে থাকে। এর ফলে গ্রামাঞ্চল এবং সমগ্র অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে উৎপাদন সম্পর্কের কোন মৌলিক পরিবর্তন না ঘটলেও শোষক শ্রেণীসমূহের সাম্প্রদায়িক চরিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ পূর্বে এই সব শ্রেণীর মধ্যে যেখানে হিন্দুদের প্রাধান্য ছিলো সেখানে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলমানদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়।
এই পরিবর্তনের ফলে অর্থনৈতিক জীবনে হিন্দুদের সাথে মুসলমানদের রেষারেষি ও প্রতিযোগিতার যে অবস্থা ছিলো তার অবসান ঘটে এবং এ অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মূল ভিত্তি দুর্বল ও শিথিল হয়। পাকিস্তান-পূর্ব যুগে বাঙলাদেশের অর্থনীতিতে শোষক শ্রেণীর মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রাধান্য যেভাবে মুসলমানদের রাজনৈতিক চিন্তাকে সাম্প্রদায়িকতার দিকে চালনা করেছিলো পাকিস্তান-উত্তর যুগে উপরোক্ত কারণে সে পরিস্থিতির মধ্যে যথেষ্ট পরিবর্তন আসে। এজন্যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পর থেকেই অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি সংগঠনের একটা প্রচেষ্টা এখানে শুরু হয়। এই প্রচেষ্টা ১৯৪৮ এবং ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে অনেকখানি শক্তি সঞ্চয় করে।
প্রত্যক্ষ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসানের পর পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বর্তমান বাঙলাদেশের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলনই হলো প্রথম সক্রিয় পদক্ষেপ এই আন্দোলনের গতি মূলতঃ এই অঞ্চলের সামন্ত সংস্কৃতির বিরুদ্ধেই নিবদ্ধ ছিলো। এর মাধ্যমেই সর্বপ্রথম ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের এক বিরাট অংশ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেন। তৎকালীন তরুণ সাহিত্যিকদের রচনার মধ্যেও এই সামন্ত বিরোধিতা অনেকাংশে প্রতিফলিত হয়।
পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামীণ ও কৃষি অর্থনীতির মধ্যে যে দ্বিতীয় পরিবর্তন আসে তা প্রথমটির মতো এতো দ্রুত না হলেও সে পরিবর্তনের চরিত্র তুলনায় অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৫০ সালের জমিদারী উচ্ছেদ আইনের দ্বারা এই পরিবর্তনের সূচনা হয় এবং তার বিকাশ ঘটে মুদ্রা অর্থনীতি ও বাজারের বিস্তৃতি, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে। মুদ্রা অর্থনীতি, বাজারের বিস্তৃতি, যোগাযোগ ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি ও শিল্পোন্নয়ন কৃষিতে পুরোদস্তুর ধনতন্ত্র প্রচলন করতে না পারলেও সামন্ত অর্থনীতির কাঠামোকে তা অনেকাংশে দুর্বল করে এবং এদেশে সামন্তবাদের ক্ষয়িষ্ণুতাকে বাড়িয়ে তোলে। এসবের ফলে গ্রামীণ ও কৃষি অর্থনীতিতে সামন্ত উৎপাদন সম্পর্কের উচ্ছেদ না হলেও সে সম্পর্ক উত্তরোত্তরভাবে শিথিল হতে থাকে।
কাজেই একদিকে শহর ও গ্রামাঞ্চলে শোষক শ্রেণীর সাম্প্রদায়িক চরিত্র পরিবর্তন (অর্থাৎ হিন্দুদের স্থান মুসলমান শোষক কর্তৃক দখল) এবং অন্যদিকে সামন্ত উৎপাদন সম্পর্ক ক্রমশঃ শিথিল হতে থাকা—পরিবর্তনের এই দুই ধারা রাজনীতিক্ষেত্রেও উত্তরোত্তর প্রতিফলিত হতে থাকে। এর ফলেই পূর্ব বাঙলার রাজনীতি ক্রমশঃ পাকিস্তান বিরোধিতার দিকে চালিত হয়। ১৯৪৮ ও ‘৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলন, ১৯৬৪-৬৫ সালের নির্বাচন, ১৯৬৮-৬৯ সালের ব্যাপক গণ- আন্দোলন ইত্যাদি এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের এক একটি পথচিহ্ন। ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচন বিজয় এবং ১৯৭১ সালে বাঙলাদেশ নামে একটি নোতুন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাও এই রাজনৈতিক পরিবর্তনেরই পরিণতি।
এখানে যে বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং বর্তমান আলোচনার মূল বিষয়বস্তু তা হলো সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র পাকিস্তান এই অঞ্চল থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বর্তমান বাঙলাদেশের সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সামন্তবাদী ধ্যান-ধারণা ও ধর্মের প্রাধান্য। এই প্রাধান্যের জন্যেই ধর্মীয় রাষ্ট্রের উচ্ছেদ, এলাকা ও ভাষাভিত্তিক একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি সত্ত্বেও বাঙলাদেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব এখনো সম্পন্ন হয়নি।
সংস্কৃতির প্রশ্নটি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উত্থাপন করার কারণ এই যে, বর্তমানে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সামন্তবাদী প্রভাব অর্থনীতি ক্ষেত্রে সামন্তবাদী প্রভাবের তুলনায় অনেক বেশী প্রবল। একমাত্র এ কারণেই বাঙলাদেশে সাম্প্রদায়িক চিন্তার এক নতুন উত্থান আমরা দেখতে পাচ্ছি, অন্য কোন কারণে নয়।
কথাটা একটু বিশদভাবে বলা দরকার। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাঙলাদেশের অর্থনীতিতে ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসের পূর্বে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছিলো সে পরিস্থিতি বিগত ছাব্বিশ বৎসরে মৌলিকভাবে না হলেও খুব তাৎপর্যপূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। শোষক শ্রেণীসমূহের মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রাধান্য এবং শোষিত শ্রেণীসমূহের মধ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রাধান্যের ফলে তৎকালীন সমাজভূমিতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র যত উর্বর ছিলো বর্তমানের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সে উর্বরতা অনেক কমে গেছে। এ জন্যেই সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে কোন রাজনৈতিক দল আজ আর এদেশে ধর্মের জিগীর তুলে পূর্বের মতো আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হবে না। কিন্তু সেটা না পারলেও সাম্প্রদায়িক চিন্তা সাধারণভাবে এদেশে যে শক্তিহীন হয়ে পড়েছে তা নয়। উপরন্তু সাম্প্রদায়িকতা বাঙলাদেশের রাজনীতিকে এখন পূর্বের থেকে অনেক সূক্ষ্মতরভাবে অগণতান্ত্রিক পথে চালনা করতে সক্ষম হচ্ছে। সাম্প্রদায়িকতার এই শক্তি ও সামর্থ্যের ব্যাখ্যা বর্তমান বাঙলাদেশের অর্থনৈতিক জীবনে যতখানি পাওয়া যাবে তার থেকে অনেক বেশী পাওয়া যাবে জনগণের সাংস্কৃতিক জীবনে। অর্থাৎ এখন এই সাম্প্রদায়িকতার উৎস সামাজিক ভিত্তিভূমিতে যতখানি, তার থেকে অনেক বেশী তার উপরিকাঠামোতে।
২
১৯৪৭ সাল থেকে, বিশেষতঃ ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের কাছাকাছি সময়ে, পূর্ব বাঙলায় ছাত্র ও শিক্ষিত যুবসমাজের একাংশের মধ্যে সামন্ত বিরোধী চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান-ধারণার সূত্রপাত হয় এবং তরুণ লেখক ও শিল্পীদের একটি ছোট গোষ্ঠী তাঁদের রচনা ও শিল্পকার্যের মাধ্যমে এই সামন্ত বিরোধিতাকে কিছুটা নির্দিষ্ট রূপদানের চেষ্টা করেন। এই প্রচেষ্টাকালে তাঁরা যে শুধু ধর্মীয় চিন্তার কাঠামোকেই ভাঙার চেষ্টা করেন তাই নয়, অন্যান্য অনেক সামন্তবাদী চিন্তা, আচার-আচরণ এবং ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই তাঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে অনেকখানি সোচ্চার হওয়ার চেষ্টা করেন। এ কাজ করতে গিয়ে ‘শিল্পের জন্য শিল্প’–এই অসৎ বুর্জোয়া ধ্বনিকেও বর্জন করে তাঁরা সাহিত্য ও শিল্প ক্ষেত্রে সমাজ ও শ্রেণী সচেতনতার ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেন।
এই সাহিত্য ও শিল্প আন্দোলনের মাধ্যমে সামন্তবাদ বিরোধিতা যেভাবে শুরু হয়েছিলো তাতে হয়তো মনে করা যেত যে, এই অঞ্চলে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সহায়ক হিসেবে তা দ্রুতগতিতে প্রবল শক্তি সঞ্চয় করবে এবং সেই শক্তি সমাজের অগণিত শোষিত মানুষের মধ্যে নিশ্চিতভাবে ছড়িয়ে পড়বে।
কিন্তু পরবর্তী বৎসরগুলিতে দেখা গেলো যে, পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে সামন্তবিরোধী বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক শিল্প-সাহিত্যের যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিলো বাস্তবতঃ তার কোন উপযুক্ত বিকাশ ঘটলো না। শুধু বিকাশ যে ঘটলো না, তা নয়। সেই সম্ভাবনা প্রায় অঙ্কুরেই বিনষ্ট হলো। যে সমস্ত লেখক-সাহিত্যিক, শিল্পীরা নোতুন পথে নোতুন উদ্দীপনায় যাত্রা শুরু করেছিলেন তাঁদের অনেকে পথ পরিবর্তন করলেন না, কিন্তু উদ্দীপনার অভাব তাঁদের প্রায় প্রত্যেকের মধ্যেই এমনভাবে দেখা দিলো যার ফলে বেশী দূর যাওয়া তাঁদের কারও পক্ষে আর সম্ভব হলো না। এর ফলে দেখা গেলো যে, পাকিস্তানী আমলে তাঁদের অনেকে ‘জাতীয় সংস্কৃতি চর্চার’ নামে ধর্মীয় সংস্কৃতির বিরোধিতা করলেন, বাঙালী সংস্কৃতির কথা বললেন, কিন্তু চব্বিশ বৎসরের সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র শাসনের অবসানের পর শিল্প সাহিত্য-সংস্কৃতির কোন ক্ষেত্রেই সামন্তবাদ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কোন বলিষ্ঠ ভিত্তি রচনা করতে তাঁরা সমর্থ হলেন না। উপরন্তু পঞ্চাশের দশকের উপরোক্ত প্রায় সব লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিকরা তো বটেই, এমনকি পরবর্তী পর্যায়ের নবীনতর লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিকরাও বিপুল সংখ্যায় কোন না কোন প্রকারে বর্তমান শোষক শ্রেণীর সেবাদাসে পরিণত হয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের অনুকূল সংস্কৃতি রক্ষা, নির্মাণ ও প্রচলনের উদ্দেশ্যে নিজেদের প্রচেষ্টাকে নিয়োজিত রাখলেন। এর ফলেই বর্তমান বাঙলাদেশে আমরা সংস্কৃতি- চর্চার নামে, গবেষণার নামে, জনগণের সংস্কৃতির নামে, যা দেখছি আসলে তা সামন্ত স্বার্থ ও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের পায়রবী ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই পায়রবী এদেশের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে যে কোন রকমেই সহায়ক হতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য। বাস্তবতঃ তা হচ্ছেও না। উপরন্তু বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিরুদ্ধে এই তথাকথিত সংস্কৃতি একটা প্রতিকূল আবহাওয়ারই সৃষ্টি করছে।
৩
পঞ্চাশের দশকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু হয়েছিলো সে আন্দোলন পরবর্তী পর্যায়ে সামন্তবাদ-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলন হিসেবে উপযুক্তভাবে বিকশিত হতে ব্যর্থ হলো কেন তার কারণ অনুসন্ধান করতে হলে মূলতঃ তা সাধারণভাবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতির মধ্যে এবং বিশেষতঃ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মে লিপ্ত ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক জীবনের মধ্যেই সন্ধান করতে হবে।
প্রথমেই বলে রাখা দরকার যে, উপরোক্ত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা সকলেই ছিলেন পেটি-বুর্জোয়া শ্ৰেণীভুক্ত। তাঁদের পরিবারের আর্থিক জীবন ভূমি মালিকানা, চাকুরী, ক্ষুদে ব্যবসা অথবা শিক্ষকতা, ওকালতী, ডাক্তারী প্রভৃতি পেশার ওপরই ছিলো প্রধানতঃ নির্ভরশীল। সে সময়ে এই অঞ্চলে শিল্প ও ব্যবসা ক্ষেত্রে বৃহৎ পুঁজি বিনিয়োগ তেমন না হওয়ার ফলে বুর্জোয়া অর্থনৈতিক বিকাশ অপেক্ষাকৃত অনেক নিম্নস্তরে ছিলো।
১৯৪৮ এবং ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে যারা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরাও ছিলেন প্রধানতঃ পেটি-বুর্জোয়া শ্ৰেণীভুক্ত। তাঁদের আর্থিক জীবন এই পর্যায়ে হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত শোষক ও প্রতিযোগীদের দ্বারা বিঘ্নিত হচ্ছিলো না, কিন্তু পাকিস্তান সরকারের বহুমুখী জাতিগত নিপীড়নমূলক নীতি তাঁদের জীবনকে নানাভাবে বিপর্যন্ত করছিলো। শুধু তাই নয়। সরকার তাঁদের সেই নিপীড়নমূলক নীতিসমূহকে ইসলামী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রক্ষার নামে বাঙলাভাষী জনগণের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছিলো এবং সেই সব নীতির প্রতিরোধকারীদেরকে ইসলাম-বিরোধী আখ্যা দিয়ে দমন করতে নিযুক্ত ছিলো। ভাষা আন্দোলনকালে এবং তার পরবর্তী বৎসরগুলিতে পূর্ব পাকিস্তানে যে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও পাকিস্তান বিরোধিতা দেখা দিয়েছিলো তা এই কাঠামোর মধ্যেই নিয়ন্ত্রিত ও বিকশিত হয়েছিলো। তৎকালে যেটুকু সামন্তবিরোধিতা দেখা দিয়েছিলো সে বিরোধিতাও এই কাঠামোর সীমা উত্তীর্ণ হতে পারেনি। অর্থাৎ এর থেকে সমাজের গভীরতর দেশে তা প্ৰবেশ করতে সক্ষম হয়নি। পঞ্চাশের দশকের আলোচ্য সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা এই অক্ষমতার মধ্যেই মূলতঃ নিহিত ছিলো।
৪
১৯৫৮ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকে আইয়ুব খানের দশ বৎসরকাল শাসনে পাকিস্তানের এই পূর্বাঞ্চলে কিছুটা পুঁজি বিনিয়োগ শুরু হয়। পশ্চিমাঞ্চলের তুলনায় পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ এখানে অনেক কম হলেও পূর্বের তুলনায় তা ছিলো অনেক বেশী। এর ফলে এই অঞ্চলে বেশ কিছু কলকারখানা গড়ে ওঠে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তৃতি ঘটে। শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যের এই বিকাশ ও বিস্তৃতি যথেষ্ট সীমিত হলেও তার ফলে পূর্ব পাকিস্তানে একটি উঠতি পুঁজিপতি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। কোন্ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই শ্রেণীটি সৃষ্টি হলো সে আলোচনা আমাদের মূল আলোচনার ক্ষেত্রে খুব প্রাসঙ্গিক।
তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের এই পুঁজি কৃষি উদ্বৃত্ত থেকে আসেনি। যেটুকু এসেছে মোট পরিমাণের তুলনায় তা নিতান্ত নগণ্য। আইয়ুব খানের ভূমিনীতি এই পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিলো। এ জন্যে তার আমলে যে ভূমিনীতি এ অঞ্চলে অনুসৃত হচ্ছিলো তারও একটা সংক্ষিপ্ত উল্লেখ এখানে দরকার।
৫
আইয়ুব খান তার তথাকথিত ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে পূর্বাঞ্চলে পরিবার প্রতি ভূমি মালিকানার সিলিং ১৯৫০ সালের জমিদারী উচ্ছেদ আইন দ্বারা নির্ধারিত একশো বিঘার থেকে তিনশো পঁচাত্তর বিঘায় তুলে দেন। এই ‘সংস্কারের’ দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার যে এখানে ভূমি কেন্দ্রীকরণকে প্রথম থেকেই উৎসাহ দিতে শুরু করেন সেটা এর থেকে বোঝা যায়। আইয়ুবের এই নীতি বস্তুতঃ তার সামগ্রিক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনারই অন্তর্গত ছিলো। এর দ্বারা একদিকে তিনি গ্রামাঞ্চলের ভূমি মালিক জোতদার শ্রেণীকে শক্তিশালী করে তাঁদেরকে তার নিজের সাথে স্বার্থের গাঁটছড়ায় বেঁধে রাখতে চেষ্টা করেন এবং অন্যদিকে পূর্ব বাঙলার শিল্পোন্নয়নকে দেশীয় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে না দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার ওপরই তাকে প্রায় সর্বতোভাবে নির্ভরশীল রাখতে সচেষ্ট হন। এর জন্য যে দুটি হাতিয়ার তিনি ব্যবহার করেন তার একটি হলো মৌলিক গণতন্ত্র, অপরটি ওয়ার্কস্ প্রোগ্রাম।
মৌলিক গণতন্ত্রের মাধ্যমে আইয়ুব খান জোতদারদের হাতে স্থানীয় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা কিছুটা হস্তান্তর করেন। এই মৌলিক গণতন্ত্রীদের অধিকাংশই ছিলো ভূমি মালিক অর্থাৎ ছোট-বড়ো জোতদার। মহাজনী কারবারও এই জোতদারদেরই হাতে মূলতঃ কেন্দ্রীভূত ছিলো। এদের হাত দিয়েই সরকার কোটি কোটি টাকা ওয়ার্কস্ প্রোগ্রামের অধীনে ব্যয় করেন। এই ব্যয়ের অধিকাংশই আবার নির্দিষ্ট হয় কাঁচা রাস্তাঘাট তৈরীর অর্থাৎ মাটি কাটার কাজে। এই মাটি কাটার কাজে যে টাকা খরচ হয় তার একটা বিরাট অংশ মৌলিক গণতন্ত্রীরা অসৎ উপায়ে আত্মসাৎ করে। রাজনৈতিক কারণে ওয়ার্কস্ প্রোগ্রামের এই টাকাকড়ির খরচ খরচার কোন অডিট অর্থাৎ হিসেব আদায়ের ব্যবস্থা করা থেকে কেন্দ্রীয় সরকার বাস্তবতঃ বিরত থাকে। এর দ্বারা একদিকে চুরিকে উৎসাহ ও প্রশ্রয় দেওয়া হয় এবং অপর দিকে মৌলিক গণতন্ত্রীদের ওপর একটা চাপও বজায় রাখা হয় এই বলে যে, তাঁদের মধ্যে কেউ গণ্ডগোল করলে অডিটের মাধ্যমে তাকে ধরা এবং শাস্তি দেওয়া হবে। ওয়ার্কস্ প্রোগ্রামের এই বিপুল ব্যয় এবং তার থেকে চুরির মাধ্যমে সঞ্চিত অর্থ জোতদাররা প্রধানতঃ জমি ক্রয় এবং মহাজনী কারবারে বিনিয়োগ করে। কারণ বর্গাদারী প্রথায় কৃষককে জমি আবাদ করতে দিয়ে ফসলের অর্ধেক ভাগ (ক্ষেত্র বিশেষে তার থেকেও বেশী) এবং ইচ্ছে মতো সুদ আদায় (শতকরা সত্তর, আশি, একশো, দুশো অর্থাৎ বেপরোয়া) এই সব অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত জোতদারদের আয়কে এমনভাবে স্ফীত করছিলো যে অন্য কোন প্রকারে তাদের সব অর্জিত ধন পুঁজি হিসেবে নিয়োগ করার চিন্তা তাদের নিষ্প্রয়োজন ছিলো। আইয়ুব সরকারও তার ভূমি নীতির মাধ্যমে ঠিক এই পরিস্থিতিই সৃষ্টি করতে চেয়েছিলো।
এখানে যে বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার তা হলো এই যে, জোতদারদের হাতে এভাবে জমি পূর্বের থেকে অনেক বেশী কেন্দ্রীভূত হলেও কৃষি অর্থনীতিতে উৎপাদন সম্পর্কের কোন মৌলিক পরিবর্তন এর দ্বারা সাধিত হলো না। উপরন্তু বর্গাপ্রথা ও মহাজনী কারবারকে জিইয়ে রাখার জন্যে শিল্পোন্নয়নের ফলে গ্রামাঞ্চলে সামন্তবাদের অবক্ষয় যত দ্রুত হওয়ার কথা ছিলো সে অবক্ষয় ততখানি দ্রুত হলো না। এদিক দিয়ে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের সাথে পশ্চিমাঞ্চলের একটা বড়ো তফাৎ ছিলো। কারণ আইয়ুবের আমলে পশ্চিম পাকিস্তানে ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে শতকরা মাত্র ২.৪ ভাগ জমি কৃষকদের কাছে হস্তান্তরিত হলেও সেই সংস্কারের প্রকৃত ক্ষেত্র ছিলো কৃষি যান্ত্রিকরণ ও বাণিজ্যিক কৃষির বিস্তার। এই দুইয়ের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানে কৃষিতে উৎপাদন সম্পর্ক যেভাবে পরিবর্তিত হয়, অর্থাৎ সামন্ত সম্পর্কের স্থানে যেভাবে সেখানে ধনবাদী সম্পর্ক স্থাপিত হতে থাকে সে রকম কোন পরিবর্তন পূর্ব পাকিস্তানে দেখা যায় না। এর মোটামুটি ফল দাঁড়ায় এই যে, কৃষি উদ্বৃত্তের অধিকাংশই সামন্ত অর্থনীতির চৌহদ্দীর মধ্যেই আটকা পড়ে। ধনবাদী অর্থনীতির সম্প্রসারণ ও শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে তা বিশেষ কোন কাজে আসে না।
৬
আইয়ুবের আমলে পূর্ব পাকিস্তানে পূর্বের তুলনায় দ্রুততর হারে যে শিল্পোন্নয়ন হয় তার পুঁজি তাহলে কোথা থেকে আসে এবং এই নোতুন ‘পুঁজিপতি’ শ্রেণীর উদ্ভব হয় কীভাবে?
আমাদের মতো কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে দেশীয় সম্পদের ওপর নির্ভর করে শিল্পোন্নয়ন করতে হলে তার প্রয়োজনীয় পুঁজি মূলতঃ কৃষি উদ্বৃত্ত থেকেই আসতে হয়। কিন্তু আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে, পূর্ব পাকিস্তানে সেই উদ্বৃত্ত প্রধানতঃ সামন্ত অর্থনীতির চৌহদ্দীর মধ্যেই আটকা ছিলো। এখানকার শিল্পোন্নয়নের পুঁজি তাহলে এলো কোথা থেকে?
এর উত্তর সহজ। এলো মূলতঃ বিদেশ থেকে। এবং বিদেশ থেকে এইভাবে আসা পুঁজির নামই সাম্রাজ্যবাদী লগ্নী পুঁজি। এই লগ্নী পুঁজিই আইয়ুবের আমলে ছিলো শিল্পোন্নয়নের মূল ভিত্তি।
একথা বলাই বাহুল্য যে, এই পুঁজি কে নিয়োগ করবে অর্থাৎ বিনিয়োগযোগ্য এই পুঁজি যাদের মধ্যে বিতরিত হবে তা নির্ধারণের মালিক ছিলো সরকার। শুধু তাই নয়, শিল্পোন্নয়নকে পুরোপুরিভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে সরকার প্রকৃতপক্ষে শিল্প লাইসেন্স, জমি, ঋণ এবং বৈদেশিক মুদ্রা এই চারটি প্রয়োজনীয় জিনিসকেই সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করতো।
১৯৫৮ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রধানতঃ আইয়ুবের এবং তারপর ইয়াহিয়ার আমলে যারা এখানকার শিল্পোন্নয়নে অংশগ্রহণ করেছিলো, কলকারখানা গড়ে তুলেছিলো, তাদের অতি অল্প সংখ্যকই ছিলো ভূমি মালিক। কিছুসংখ্যক ছিলো ঠিকাদার যারা ১৯৪৭ সাল থেকে এদেশে ঠিকাদারী কারবার করে কিছু পুঁজি সঞ্চয় করেছিলো, তারা অনেকে এই পুজি আইয়ুবের আমলে শিল্পক্ষেত্রে নিয়োগ করে। কিন্তু ব্যাপকভাবে যারা শিল্প গঠন কাজে নিযুক্ত হলো, যারা হলো অধিকাংশ, তারা কেউই ভূমি মালিক অথবা ঠিকাদার ছিলো না। তাঁরা এমন ব্যক্তি ছিলো যারা পারিবারিক অথবা ব্যক্তিগত সূত্রে শাসক দল অথবা ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী ও আমলাদের সাথে সম্পর্কিত। এই সম্পর্কের ভিত্তিতে তাঁরা সরকারের থেকে শিল্প স্থাপনের লাইসেন্স পেলো, জমি পেলো, পেলো ঋণ ও বৈদেশিক মুদ্রা। অর্থাৎ সহজ কথায় বলা চলে যে, এদেশের শিল্পোন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে যারা এগিয়ে এলো, অথবা আসার সুযোগ পেলো, তারাও মোটামুটিভাবে গ্রামাঞ্চলের জোতদার, মহাজন, মৌলিক গণতন্ত্রীদের মতো আইয়ুব শাসনের সাথে একই গাঁটছড়ায় বাঁধা থাকলো।
৭
কৃষি অর্থনীতি এবং শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে উপরোক্ত পরিস্থিতির ফলে পূর্ব বাঙলায় একদিকে যেমন ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত ব্যবস্থাকে যথাসাধ্য টিকিয়ে রাখা হলো, অন্যদিকে তেমনি পুঁজির বিকাশকে রাখা হলো সাম্রাজ্যবাদী লগ্নী পুঁজির ওপর নির্ভরশীল করে। এই কারণে এখানে কোন উল্লেখযোগ্য স্বাধীন পুঁজিপতি শ্রেণীর জন্ম হলো না। হওয়ার কথাও নয়। এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদী ও নয়া উপনিবেশবাদী দেশগুলির সর্বত্র এই অবস্থাই মূলতঃ বিরাজ করছে।
আইয়ুবের আমলে যারা শিল্পসাহিত্য চর্চা করতো এবং বুদ্ধিজীবী হিসেবে গণ্য হতো তারা কোন স্বাধীন শ্রেণীর লোক ছিলো না। তারা ছিলো এমন এক মধ্যশ্রেণীভুক্ত যে শ্রেণীর আর্থিক জীবন ওপরে বর্ণিত আর্থিক কাঠামোরই অন্তর্গত ছিলো। সেদিক দিয়ে তাঁদের শ্রেণীগত দুর্বলতার অন্ত ছিলো না।
এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে, তাকে আরও বাড়িয়ে তুলে, বুদ্ধিজীবী ও শিল্পী সাহিত্যিকদেরকে যথাসাধ্য নিজেদের অনুগত ও সহায়ক শক্তি হিসেবে ব্যবহারের জন্যে আইয়ুবের আমলে ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ কাজ করতে গিয়ে আইয়ুব সরকার সাংবাদিক ও কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপরই নির্ভর করে বেশী। অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য লেখক,
শিল্পী ও বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক ও শিক্ষক মহল থেকে এলেও এঁদের কিছু অংশ অন্যান্য জীবিকায়ও নিযুক্ত ছিলেন। সরকার এঁদেরকেও উপেক্ষা করলেন না। এঁদের মাহিনা বৃদ্ধি ও বাসস্থানের উন্নতি তো হলোই, উপরন্তু শিক্ষার ব্যবস্থা, বিদেশ ভ্রমণ ইত্যাদির পথও সুগম ও প্রশস্ত করা হলো। এর সাথে যুক্ত হলো সরকারী উদ্যোগে নানান ‘সাহিত্যকর্ম’ করে প্রচুর অর্থ লাভের ব্যবস্থা এবং সাহিত্য ও শিল্পকর্মের জন্যে খেতাব ও পুরস্কার। লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদেরকে পুরস্কার বিতরণ করতে শুধু সরকারই নয়, পাকিস্তানের বৃহৎ পুঁজিও এগিয়ে এলো। দাউদ, আদমজী, ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক প্রভৃতির পুরস্কারের মালা অনেক ‘কৃতী’ ব্যক্তির গলাতেই ঝুলতে লাগলো। আইয়ুবের আমলে এই মালা গলায় ঝুলিয়েই অনেকে আইয়ুব শাসনের এবং ‘বাইশ পরিবারের’ বিরুদ্ধে জেহাদে নামলেন!
এতেও আশ্চর্য হওয়ার কিছুই ছিলো না। কারণ ঠিক ঐ সময়েই অনেক দেশবরেণ্য নেতা কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার ও ‘বাইশ পরিবারের’ বিরুদ্ধে মাঠে ঘাটে জেহাদ ঘোষণা করে বেড়ালেও দাউদ, আদমজী, হারুণদের অর্থেই তাঁরা নিজেদের পরিবার প্রতিপালন করছিলেন। লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেতা পর্যন্ত এই শ্রেণীর লোকদের শ্রেণীগত চরিত্রই ছিলো তাই।
৮
ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী লগ্নী পুঁজির এই অবস্থানের জন্যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যথার্থভাবে সামন্ত সংস্কৃতির বিরোধী কোন গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল সংস্কৃতি যে পেটি-বুর্জোয়া সাহিত্য ও সংস্কৃতি কর্মীদের দ্বারা যথাযথভাবে বিকশিত হবে না তা বলাই বাহুল্য। এজন্যেই দেখা যায় যে, পঞ্চাশের দশকের শুরুতে এই শ্রেণীর সাহিত্য ও সংস্কৃতি কর্মীরা যে সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার সূত্রপাত করেছিলেন তা ষাটের দশকেও দানা বাঁধলো না। উপরন্ত ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত ও মুৎসুদ্দী সংস্কৃতি হিসেবেই তার পরিচয় উত্তরোত্তর পরিস্ফুট হলো। বাঙলাদেশের এই পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীর ‘সংস্কৃতি চর্চা’ ১৯৭১ সালের পর থেকে যে মোড় নিয়েছে তার চরিত্র আরও ভয়াবহ। কারণ এই সংস্কৃতি যে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত সংস্কৃতিকে আঘাত হানতেই শুধু অপারগ তাই নয়। সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশের ফলে এই সংস্কৃতি আজ মধ্যবিত্ত সমাজের সর্বস্তরে এবং সেই সাথে দেশের প্রায় সমগ্র বুদ্ধিজীবী মহলে যে নৈরাজ্য বিস্তার করছে তা সব দিক দিয়ে সামন্ত সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার পক্ষেই সর্বতোভাবে সহায়ক হচ্ছে।
এই পরিস্থিতিও অকারণে সৃষ্টি হয়নি। সেজন্যে এর যথার্থ কারণটি বোঝার জন্যে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের পর বাঙলাদেশের অর্থনৈতিক জীবনে কি পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তার সাথে আমাদেরকে পরিচিত হতে হবে।
পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সামন্ত স্বার্থ ও পুঁজি স্বার্থের সাথে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের একটা ঘনিষ্ঠ যোগ ছিলো। এজন্যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার ও বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর নিপীড়নের বিরুদ্ধে যারা রাজনীতিগতভাবে সংগঠিত হচ্ছিলো, পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের জন্যে যারা রাজনীতিগতভাবে সোচ্চার ছিলো এবং পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার রাজনৈতিক ধ্বনি যারা তুলেছিলো, তাঁদের সাথে এদেশের সামন্ত স্বার্থ অথবা উঠতি পুঁজিপতিদের (যারা মূলতঃ ছিলো মুৎসুদ্দী চরিত্রের) অনেক দিন পর্যন্ত কোন ঘনিষ্ঠ যোগ ছিলো না। সামন্ত স্বার্থ ও বাঙালী পুঁজিপতিদের সাথে তাদের এই যোগ স্থাপিত হয় মোটামুটিভাবে ১৯৬৮-৬৯ সালের ব্যাপক গণ-আন্দোলনের পর থেকে। কিন্তু যোগ স্থাপিত হলেও এই রাজনৈতিক লক্ষ্যের প্রতি সমর্থনে তাঁরা ১৯৬৯, এমনকি ১৯৭০ সাল পর্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ত ছিলো। এ দ্বিধা তাদের ঘোচে ১৯৭১ সালের গোড়ার দিকে, বিশেষ করে মার্চ মাসের দিকে। উচ্চ শ্রেণীর বাঙালী আমলারাও ছিলো কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নির্ভরশীল এবং তাদের অনুগত। তাদেরও এই নির্ভরশীলতা এবং আনুগত্য ১৯৭১ সালেই অনেক শিথিল হয়ে পড়ে এবং তারাও অন্যান্যদের সাথে দেশপ্রেমিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। কিন্তু ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত স্বার্থ, মুৎসুদ্দী বাঙালী পুঁজি ও আমলাতন্ত্রের এই আনুগত্য পরিবর্তন এতো দেরীতে ঘটেছিলো যে তাঁরা এদেশের সর্বপ্রধান ও সব থেকে প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের মধ্যে কোন শক্তিশালী স্থান অধিকার করতে পারেনি।
শুধু এই কারণেই যে আওয়ামী লীগের মধ্যে এই সমস্ত শ্রেণীর স্বার্থ শক্তিশালী হতে পারেনি তাই নয়। এর আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিলো। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ ইয়াহিয়ার সামরিক সরকার যখন এই অঞ্চলের জনগণের ওপর জাতিগত নিপীড়নকে একটা চরম পর্যায়ে নিয়ে গেলো এবং তাদের ওপর এক সর্বাত্মক সামরিক আক্রমণ শুরু করলো তখন শ্রেণীগতভাবে এরা তার বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধে অংশগ্রহণ করতে পারলো না। এদের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে কিছু কিছু ব্যতিক্রম দেখা গেলেও এরা হয় সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় থাকলো, নয় কিছুটা সহযোগিতা করতে নিযুক্ত হলো। ‘দেশপ্রেমিক’ আওয়ামী লীগওয়ালারা দেশত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিলেও এরা পূর্ব পাকিস্তানে থেকে গেলো। এই সবের ফলে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পরবর্তী পর্যায়ে ভারতের মাটি থেকে যে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক নেতৃত্বে পাকিস্তানী সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালিত হলো সে আওয়ামী লীগের মধ্যে বিপুল প্রাধান্য থাকলো পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীর। এই শ্রেণীর অন্তর্গত হলো ব্যবসায়িক মধ্যস্বত্বভোগী ফড়িয়া শ্রেণী, ছাত্র এবং যুবক দল। এরা শ্রেণীগতভাবে ছিলো নিতান্ত দুর্বল। এবং তাদের দুর্বলতার মূল কারণ নিহিত ছিলো উৎপাদনের সাথে তাদের সম্পর্কহীনতায়।
ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কর্তৃত্বাধীনে এই অঞ্চলে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে উৎপাদনের সাথে সম্পর্কহীন পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর এই অংশের হাতেই রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের পর থেকে লুটতরাজের যে অবাধ লীলা-খেলা বাঙলাদেশে শুরু হয়েছে তার ব্যাখ্যা এই পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীর ক্ষমতা দখলের মধ্যেই পাওয়া যাবে। একথার অর্থ আবার এই নয় যে, ১৯৭১ সালে ছাত্র ও যুব সমাজের যে অংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলো তারা সকলেই চরিত্রগত দিক দিয়ে সমাজবিরোধী ছিলো। মোটেই তা নয়। এদের এক বিরাট অংশ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে যুদ্ধে নেমেছিলো এবং এই অঞ্চলে একটি শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই তারা অনেকে জীবনপণ করেছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও যুদ্ধকালে এবং যুদ্ধোত্তর পর্যায়ে তারা উল্লেখযোগ্য কোন প্রভাব ঘটনাপ্রবাহের ওপর বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি।
ছাত্র ও যুবসমাজের এই ব্যর্থতার কারণ রাজনীতিক্ষেত্রে তারা প্রধানতঃ উপরোক্ত বিভিন্ন ধরনের মধ্যস্বত্বভোগী ফড়িয়া শ্রেণীর সাথেই যুক্ত ছিলো এবং তারা নিজেরা ছিলো সম্প্রদায়গতভাবে উৎপাদনের সাথে অধিকতর সম্পর্কহীন। তাদের এই সামাজিক অবস্থান শুধু যে বিরাট সংখ্যক দেশপ্রেমিক ছাত্র ও যুবকদেরকে ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বরের পরবর্তী পর্যায়ে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছিলো তাই নয়। তাদের অনেককেই এই ফড়িয়া শ্রেণীর লুটতরাজের আবর্তের মধ্যে আকর্ষণ করে পরিণত করেছিলো সমাজবিরোধী শক্তিসমূহের অংশে। ফড়িয়াদের সাথে সাথে এই ধরনের ছাত্র ও যুবকদের সমাজবিরোধী কার্যকলাপ এখনো পর্যন্ত এই দেশে অব্যাহত আছে। শুধু তাই নয়। এই ছাত্র যুবকদের একটা অংশ নিজেরাই এখন পরিণত হয়েছে ব্যবসায়ী মধ্যস্বত্বভোগী ফড়িয়াতে।
৯
আওয়ামী লীগের মধ্যে সংগঠিত এই ফড়িয়া শ্রেণী প্রথম দিকে অবাঙালীদের ও পাকিস্তান সামরিক সরকারের সহযোগী বাঙালীদের একাংশের (অপর অংশ সুকৌশলে ত্বরিৎগতিতে আওয়ামী লীগের মধ্যেই ঢুকে পড়ে) স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি খোলাখুলিভাবে লুটতরাজ করে। এই প্রাথমিক পর্বের পর সমাজতন্ত্রের ধ্বনি তুলে এরা বাংলাদেশের শিল্পবাণিজ্য স্বার্থের শতকরা প্রায় পঁচাশি ভাগের ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপন করে সেগুলিকেও ব্যক্তিগত ধনসম্পদ বৃদ্ধির কাজে যথাসাধ্য ব্যবহার করে। উৎপাদনের সাথে যেহেতু এই শ্রেণীর লোকদের কোন সম্পর্ক কোন দিন ছিলো না, কাজেই উৎপাদনের থেকে চোরাকারবার, চোরাচালান, লাইসেন্স, পারমিট এবং মওজুদ সম্পদের অবাধ লুটতরাজের মাধ্যমে ধন বৃদ্ধিই হয় তাদের মৌলিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অনুসরণ করে তারা ভৌতিকভাবে নিজেদের ধনসম্পদ বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক অদৃষ্টপূর্ব নৈরাজ্যের সৃষ্টি করে। এই নৈরাজ্যের অবসান বাঙলাদেশে এখনো ঘটেনি।
১০
এই সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর সংস্কৃতি চর্চার চরিত্র যে কি দাঁড়াবে তা বলাই বাহুল্য। আজকের বাঙলাদেশে এই লাগামহীন মধ্যশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিরা সংস্কৃতি চর্চা, গবেষণা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলনের নামে যা করছে তার কোন গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল চরিত্র তো নেই, উপরন্তু সাম্রাজ্যবাদের অভিপ্রেত এক ধরনের অপসংস্কৃতি এদেশে সৃষ্টি ও আমদানী করে এরা সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও সামাজিক নৈরাজ্যেরই প্রতিফলন ঘটাচ্ছে এবং তাকে বাড়িয়ে তুলতে সর্বতোভাবে সাহায্য করছে। জনগণের দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে একটা ভণ্ডামিপূর্ণ হাহুতাশ সৃষ্টি এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণতাকেই যে এই অপসংস্কৃতি মূল অবলম্বন হিসেবে আঁকড়ে ধরবে তাতেও তাই আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই পরিস্থিতির জন্যে বাঙলাদেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ বর্তমান পর্যায়ে ঘটছে না। এ বিকাশ ঘটাতে গেলে সাংস্কৃতিক কর্মীরদেরকে একদিকে সামন্ত সংস্কৃতি এবং অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা উৎসাহিত ইন্দ্রিয়কেন্দ্রিক অপসংস্কৃতি – এ দুয়েরই বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রামের প্রয়োজন। কিন্তু যে পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্য এবং সংস্কৃতি কর্মীরা আজ সামগ্রিক লুটতরাজের অংশীদার, বাড়ী, গাড়ী, বিষয় সম্পত্তির হঠাৎ-মালিক, যোগ্যতার তুলনায় অনেক উচ্চতর চাকুরিজীবী ও লাইসেন্স পারমিটের কারবারী হওয়ার অভিলাষী, বিদেশ ভ্রমণ ও ভোগবিলাসের বিবিধ উপকরণের চিন্তায় আকণ্ঠ নিমগ্ন, তারা যে শুধু সেই সংগ্রামে আজ অংশ গ্রহণ করছে না তাই নয়। তারা এই লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধেই নিজেদের সমস্ত কর্মকাণ্ডকে পরিচালনা করতে নিযুক্ত এবং সংকল্পবদ্ধ রয়েছে।
১১
বাঙলাদেশের পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি কর্মীদের এই অবস্থা যেমন একটি বাস্তব সত্য তেমনি অন্যদিকে আর একটি বাস্তব সত্য এবং এই যে, এই শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতিকর্মীদের ভূমিকা যতদিন পর্যন্ত না তাৎপর্যপূর্ণভাবে এবং আমূলভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত এ দেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হবে না। শুধু তাই নয়। ততদিন পর্যন্ত এ কথা বলা ভুল হবে যে, এ দেশে চমৎকার বিপ্লবী পরিস্থিতি বিরাজ করছে।
ঐতিহাসিক বস্তুবাদের একটি মূল সূত্রকে অস্বীকার করে কেউ যদি প্রবলভাবে এবং ক্রমাগত চিৎকার করে যান যে, বাঙলাদেশে এই মুহূর্তে চরম বিপ্লবী পরিস্থিতি বিরাজ করছে তাহলে তার দ্বারা কোনো দৈব প্রক্রিয়ার বিপ্লবী পরিস্থিতি সৃষ্টি ও বিপ্লব সম্পন্ন হবে না। তার ফল এই দাঁড়াবে যে, বিপ্লব সম্পর্কে কতকগুলি বিভ্রান্তিকর বক্তব্য উপস্থিত করে এমন সব রণনীতি ও কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হবে যা বিপ্লবের বিরুদ্ধে ও পরিপন্থী শক্তিসমূহকেই জোরদার করবে। ১৯৪৮ সাল থেকে এই দেশে বস্তুতঃ তাই ঘটে আসছে। এ জন্যে সেই সময় থেকেই বিপ্লবী পরিস্থিতি চমৎকার এই বাক্যটি শত শত বিপ্লবী পুস্তিকা ও ইস্তাহারে মুদ্রিত ও প্রচারিত হলেও এদেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব তো নয়ই, এমন কি শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবও ঘটেনি। লক্ষ লক্ষ বিপ্লবী কর্মীর জীবন বিনষ্ট, বিপন্ন ও বিপর্যস্ত হয়েছে মাত্র।
এ কারণেই আজ প্রয়োজন কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস বিশেষভাবে পর্যালোচনা করা এবং সেই পর্যালোচনার ক্ষেত্রে দেখার চেষ্টা করা যে আমাদের দেশের মতো একটি দেশে কমিউনিস্ট নেতৃত্বে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিস্থিতি সৃষ্টি ও সেই বিপ্লবকে সম্পন্ন করার জন্যে যা কিছু করণীয় তা এতদিন যথার্থভাবে করা কমিউনিস্টদের দ্বারা সম্ভব হয়েছে কিনা। বর্তমান আলোচনায় আমরা সামন্ত সংস্কৃতির বিলোপ সাধনের ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের ভূমিকা সম্পর্কে কিছুটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো, কারণ যে কোন ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদ কবলিত দেশে কমিউনিস্টদের এই ভূমিকা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। এই ভূমিকার মাধ্যমেই তাঁরা যে শুধুমাত্র সেই বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সহায়ক হয় তাই নয়, তাতে তাঁরা শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে নেতৃত্বের স্থানে অধিষ্ঠিত হয়।
১২
পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে সামন্ত সংস্কৃতির বিরুদ্ধে অল্পসংখ্যক শিল্পী সাহিত্যিকরা যে সীমিত আন্দোলন শুরু করেন তাতে কমিউনিস্ট পার্টি, নিজেরা দুর্বল হলেও, কিছুটা সহায়তা করে। শুধু শিল্প-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নয়, রাজনীতি ক্ষেত্রেও কমিউনিস্টরা এই সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসেন। বস্তুতপক্ষে তাঁদের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতার ফলেই পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ অল্পদিনের মধ্যেই তৎকালীন অবস্থায় মোটামুটি একটা শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে দাঁড়াতে সক্ষম হয়।
১৯৫১ সালের মার্চ মাসে প্রতিষ্ঠিত এই পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ প্রায় প্রথম থেকেই রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দুই ক্ষেত্রেই অনেকখানি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে যুবলীগের নেতা ও কর্মীরাই মূলতঃ নেতৃত্ব দান করেন এবং সে সময়ে অনেক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সামন্ত-বিরোধী এক নোতুন আবহাওয়া সৃষ্টির প্রচেষ্টা তাঁরা চালান।
কিন্তু ১৯৫৮ সালের সামরিক অভ্যুত্থান পর্যন্ত কোন রকমে টিকে থাকলেও ১৯৫৬ সালের পরবর্তী বছরগুলোতে যুবলীগের রাজনৈতিক তৎপরতা ক্রমশঃ কমে এসে পরে প্রায় বন্ধ হয়ে যায় এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও সংগঠনটি কোন অগ্রগতি সাধন করতে পারে না। পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের এই পরিণতি মূলতঃ তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা অনুসৃত নীতির ফলেই ঘটেছিলো।
কি সেই নীতি? নীতিটি হলো আওয়ামী লীগের মধ্যে ‘অনুপ্রবেশ’ করে সেই রাজনৈতিক সংগঠনটিকে অধিকতর প্রগতিশীল’ করা এবং সেই সাথে নিজেদের গণসংযোগ বৃদ্ধি করা। পূর্বে যুবলীগের মতো একটি ফ্রন্টের মাধ্যমে যে কাজ হচ্ছিলো তার ফলকে যথেষ্ট মনে না করে অথবা ব্যাপক শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের মাধ্যমে তাকে আরও প্রসারিত করার চেষ্টা না করে তারা আওয়ামী লীগের মধ্যে অনুপ্রবেশ করার নীতি গ্রহণ করার পর যুবলীগের রাজনৈতিক কর্মসূচী কমিয়ে দেওয়া হয়। শুধু কমিয়ে দিয়ে নয়, রাজনৈতিক কর্মসূচী প্রায় বাতিল করে তাকে তাঁরা পরিণত করেন কেবলমাত্র একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে। কিন্তু যুবলীগের সৃষ্টি শুধু সাংস্কৃতিক কাজের জন্যে হয়নি। রাজনৈতিক কাজই ছিলো তার মূল উদ্দেশ্য। সংগঠনের কাঠামোও সেইভাবে তৈরী হয়েছিলো। কাজেই সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর মধ্যে যুবলীগের কর্মীরা নিজেদের কাজ সীমাবদ্ধ রেখে যখন রাজনৈতিক কাজের জন্যে আওয়ামী লীগের মধ্যে প্রবেশ করলেন তখন সেই সংগঠনটি ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেলো। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দুই কাজ থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যুবলীগ ১৯৫৮ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের সময় বিলুপ্ত হলো কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির মতো আর পুনরুজ্জীবিত হলো না।
সামন্ত সংস্কৃতির বিরুদ্ধে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠিত উদ্যোগ কিছুটা যুবলীগের মাধ্যমেই হয়েছিলো। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টিই সেই সংগঠনটিকে শেষ করলো এবং তার পরিবর্তে অন্য কিছু তারা খাড়া করতে পারলো না। গণতন্ত্রী দল নামে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান অনেকটা তাদের উদ্যোগেই ১৯৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। এই গণতন্ত্রী দল, আওয়ামী লীগ এবং এবং তারপর ১৯৫৭ সাল থেকে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি নিজেদের অধিকাংশ শক্তিকে নিয়োজিত রেখে পেটি-বুর্জোয়া রাজনীতির পুষ্টি সাধন করলো কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি হিসেবে সামন্ত সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এবং দেশীয় শ্রেণী শত্রুদের বিরুদ্ধে পার্টিগতভাবে নিজেদের শক্তিকে বৃদ্ধি করতে তারা পারলো না।
তাদের এই অক্ষমতার কারণ তৎকালীন পার্টির এবং পরবর্তীকালে একাধিক বিভক্ত পার্টির মধ্যে পেটি বুর্জোয়া ধ্যান-ধারণা ও সংশোধনবাদের প্রায় অনিয়ন্ত্রিত প্রভাব। এই জন্যই কমিউনিস্ট পার্টি পেটি বুর্জোয়া রাজনৈতিক পার্টিগুলির মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে গিয়ে পেটি- বুর্জোয়া পার্টিগুলিকে অধিকতর প্রগতিশীল করতে পারেনি, নিজেরাই পরিণত হয়েছে অধিকতর পেটি-বুর্জোয়া পার্টিতে। শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি বিভিন্ন ফ্রন্টের মাধ্যমে গণসংযোগ স্থাপন করতে পারে, সামন্তবাদ ও সামাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে পারে, কিন্তু অন্য শ্রেণীর একটি রাজনৈতিক পার্টির মধ্যে অনুপ্রবেশ করে তার চরিত্র যে পরিবর্তন করতে পারে না তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির অথবা পরবর্তীকালের একাধিক পার্টির ইতিহাসই তা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে।
১৩
কমিউনিস্ট পার্টির উপরোক্ত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচী অর্থাৎ পেটি-বুর্জোয়া রাজনৈতিক পার্টির মধ্যে পার্টি সদস্যদেরকে ঢুকিয়ে বৃহত্তর গণসংযোগের চেষ্টা (যা প্রকৃতপক্ষে সংশোধনবাদী সুবিধাবাদেরই নামান্তর ছিলো) সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও কমিউনিস্টদের ভূমিকাকে প্রায় শূন্যের কোঠায় নামিয়ে এনেছিল। এর ফলে ব্যাপক জনগণের মধ্যে শ্রমিক, কৃষক, নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীসমূহের মধ্যে কোন সাংস্কৃতিক আন্দোলন তারা সৃষ্টি করতে পারেনি। এদেশে যে সামন্ত সংস্কৃতি প্রতিক্রিয়ার দুর্গ হিসেবে এখনো বিরাজ করছে, যে সংস্কৃতি সাম্প্রদায়িকতা থেকে শুরু করে হাজারো সমাজবিরোধী ও প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারা ও কর্মকাণ্ডের জন্মদান করছে, তার বিরুদ্ধে কোন সংগঠিত আন্দোলন করতেও তারা সমর্থ হয়নি।
তাদের এই ব্যর্থতার কারণ তৎকালীন পাকিস্তানে বৃহৎ পুঁজি ও কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে এদেশে যে প্রতিরোধ আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিলো সে আন্দোলনের নেতৃত্ব শ্রেণীগতভাবে ছিলো পেটি-বুর্জোয়াদের হাতে। এই শ্রেণীর রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীরাই সে আন্দোলনের চরিত্র এবং দিক নির্ণয় করেছিলেন। এ সব ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির কোন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভূমিকা না থাকায় অথবা সে ভূমিকা নির্ধারণ করতে তারা সক্ষম না হওয়ায় সংস্কৃতি ও রাজনীতি ক্ষেত্রে পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রাধান্যই শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। কমিউনিস্টদের ভূমিকা সেখানে থাকে অপেক্ষাকৃত অনেক গৌণ।
এ প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের উল্লেখ খুবই প্রাসঙ্গিক এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয়। স্বল্পকাল স্থায়ী লেখক ও শিল্পী সংঘ (কমিউনিস্টদের দ্বারা পরিচালিত ও ইংরেজ আমলে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটির পূর্ব পাকিস্তান শাখা বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি এবং অচিরেই তা বিলুপ্ত হয়েছিলো) ও যুবলীগ ব্যতীত পূর্ব পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পরিচালিত অথবা প্রভাবাধীন এমন কোন প্রতিষ্ঠানই থাকেনি যার মাধ্যমে এদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন অগণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনকে তারা একটা সুষ্ঠু সাংগঠনিক চরিত্র দান করতে পারতো। শুধু তাই নয়। যে পেটি বুর্জোয়ারা শ্রেণীগতভাবে আলোচ্য পর্যায়ে উপরোক্ত আন্দোলনে নেতৃস্থানে অধিষ্ঠিত থাকে তারাও নিজেদের এমন কোন প্রতিষ্ঠান খাড়া করতে পারেনি যার মাধ্যমে তারা কোন সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে একটা দৃঢ় কাঠামোর মধ্যে রেখে পরিচালনা করতে পারতো।
এজন্যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে অর্থাৎ পূর্ব বাঙলায় মাঝে মাঝে সাংস্কৃতিক আন্দোলন কিছুটা জোরদার হয়ে উঠলেও সেই আন্দোলনকে একটানাভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা কমিউনিস্ট পার্টি অথবা পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীর কারও পক্ষেই সম্ভব হয়নি। মাঝে মাঝে যখন কোন গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক অধিকার খর্ব অথবা হরণ করার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার বা তার তাঁবেদার প্রাদেশিক সরকারের পক্ষ থেকে কোন বিশেষ হামলা এসেছে তখনই সেই হামলার বিরুদ্ধে অবস্থা বিশেষ প্রতিরোধ কম-বেশী সংগঠিত হয়েছে— যেমন ভাষা নিপীড়নের ক্ষেত্রে, শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের ওপর নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে, প্রগতিশীল বইপত্র বাজেয়াপ্তকরণের ক্ষেত্রে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সরকার বৃহৎ পুঁজি ও সামন্ত স্বার্থের দ্বারা সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পিত নীতিসমূহের একটানা আক্রমণের বিরুদ্ধে কোন একটানা সুষ্ঠু ও সংগঠনগত প্রতিরোধ সৃষ্টি এদেশে কারও দ্বারা সম্ভব হয়নি। পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর এই অক্ষমতার কারণ তাদের নিজস্ব শ্রেণীচরিত্র এবং পূর্ব বাঙলায় তাদের বিশেষ অবস্থানের মধ্যেই নিহিত ছিলো। শ্রেণী হিসেবে তাঁদের মধ্যে ফড়িয়া চরিত্র লক্ষণসমূহ খুব বেশী প্রবল থাকাতেই তারা মেরুদণ্ডহীন অবস্থায় বিরাজ করতো এবং সেই অবস্থার ফলেই তারা সংস্কৃতি ক্ষেত্রে কোন সুষ্ঠু অথবা সংগঠনগত প্রতিরোধের জন্মদান করতে পারেনি। তৎকালীন পরিস্থিতিতে গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনসমূহের কাঠামোগত দুর্বলতা বরাবরই বর্তমান ছিলো।
১৪
পূর্ব বাঙলার গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মূল নেতৃত্ব শ্রেণীগতভাবে ফড়িয়া চরিত্র সম্পন্ন পেটি-বুর্জোয়াদের হাতে ন্যস্ত থাকায় সেই আন্দোলন কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত হলেও সরাসরি ও প্রবলভাবে তা কখনো সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়নি। উপরন্তু সংস্কৃতিক্ষেত্রে বাঙালী-অবাঙালী প্রশ্নকে সামনে এনে তারা এদেশে সামন্ত সংস্কৃতি এবং সংস্কৃতিক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশকে সুকৌশলে প্রশ্রয় দিয়েছিলো
এই প্রশ্রয় তাঁরা অকারণে দেয়নি। তাদের শ্রেণী চরিত্র বিশ্লেষণ করলে এবং তাঁদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডকে বিচার করলে দেখা যাবে যে পূর্ব বাঙলার এই পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণী প্রধানতঃ ফড়িয়া চরিত্র লক্ষণসম্পন্ন হলেও সেই চরিত্র কাঠামোর মধ্যে দুটি বিশেষ ও নির্দিষ্ট ধারা বিরাজ করেছিলো। এর মধ্যে একটি ছিলো সামন্ত ভাবিত এবং অপরটি বাহ্যতঃ সামন্তবিরোধী। এই দ্বিতীয় ধারাটিকে ‘বাহ্যতঃ’ সামন্তবিরোধী বলা হচ্ছে এ জন্যে যে আসলে তা ছিলো সাম্রাজ্যবাদ প্রভাবিত অর্থাৎ মুৎসুদ্দী চরিত্রের এবং সে কারণেই মূলতঃ সামন্তবাদ বিরোধী নয়।
ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রথম ধারার অন্তর্গত ব্যক্তিরা উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত লাভ করে এবং সোফা সেট, রেডিওগ্রাম, টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটার নিয়ে ঘরকন্না করলেও মাথায় টুপি দিয়ে গাড়ী হাঁকিয়ে শুক্রবার দিন মসজিদে পরম ভক্তের মতো নামাজ পড়তে যেতেন, রোজার মাসে উপবাস করতেন, ভিক্ষুককে খয়রাত দিতেন, বিভিন্ন পীরের দরগায়, এমনকি বেলতলা বটতলার সাধু-সন্ন্যাসী পীর ফকিরদের আস্তানায় পর্যন্ত ধর্না দিতেন। অন্যদিকে, দ্বিতীয় ধারার অন্তর্গত ব্যক্তিরা নামাজ-রোজার ধারে কাছে না গিয়ে সুরা পান করে, তিন পাত্তি ও হাউজি খেলে যৌন ব্যাভিচার চালিয়ে, ধর্ম ও ধর্মপুরুষদের বিরুদ্ধে নির্বোধ আস্ফালন এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকর হয় এমন সব মন্তব্য করে বেড়িয়ে দিবারাত্রি যাপন করতেন। সমগ্র পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যেই এই দুই ধারা বর্তমান থাকলেও অল্পসংখ্যক ব্যক্তি অবশ্য এই দুই ধারারই বাইরে ছিলো অথবা এই দুই ধারারই অল্পবিস্তর সংমিশ্রণ নিজেদের চরিত্রে ঘটিয়েছিলো।
১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের পর থেকে অর্থাৎ পূর্ব বাঙলায় বাঙলাদেশ নামে একটি পৃথক রাষ্ট্র স্থাপিত হওয়ার পর থেকে এই অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন তো হয়ই নি, উপরন্তু দ্রুত অবনতি ঘটেছে। যে ফড়িয়ারা আজ বাঙলাদেশে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তাদের উপযুক্ত সংস্কৃতিই এদেশে এখন বিকশিত হচ্ছে। কালোবাজার, চোরাচালান, লাইসেন্স পারমিট, লুটতরাজ যে সমাজের ব্যবসা বাণিজ্য ও ধনসম্পদ আহরণের একটা মৌলিক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা যায়, সে সমাজে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় গবেষণা ও সংস্কৃতিচর্চাকারীরাও যে একই চরিত্রসম্পন্ন হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এখানে স্বভাবতই তাই হচ্ছে।
এ ধরনের ‘গবেষণা’ ও ‘সংস্কৃতিচর্চা’ যারা করছে পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীর অনেকেই ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের সমালোচনা করেন। এভাবে সমালোচনা প্রায় সব ক্ষেত্রেই সমাজসচেতন সমালোচনা না হয়ে পেটি-বুর্জোয়া পরচর্চাতেই পর্যবসিত হয়। কারণ এই সব সমালোচকরা ব্যক্তিগতভাবে কোন কোন ‘গবেষক’, ‘মহাগবেষক’ অথবা সংস্কৃতি সেবীদের সম্পর্কে তীক্ষ্ণ ধারালো মন্তব্য করলেও, তারা যে তাদের অধিকৃত পদসমূহের সম্পূর্ণ অযোগ্য একথা তাদের সমালোচনার মধ্যে উল্লেখ করলেও উল্লিখিত গবেষক ও সংস্কৃতিসেবীদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে তারা কোন সমালোচনার মধ্যে যান না বা অনেকক্ষেত্রে সচেতনভাবে যেতে চান না। তারা শুধু বলেন, অমুক লোকটি গবেষক, মহাগবেষক, সংস্কৃতিসেবী বলে নিজেকে দাবী করলেও আসলে মূর্খ, মহামূর্খ অথবা বেড়াল তপস্বীর মতো সংস্কৃতিসেবী অর্থাৎ সংস্কৃতির ঘাতক। কিন্তু তারা জানার চেষ্টা করেন না, জানতে চান না অথবা জেনেও একথা বলতে চান না যে, কি ধরনের সমাজব্যবস্থা এই ধরনের নিকৃষ্ট ব্যক্তিদেরকে গবেষণা ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার উপযুক্ত পাত্র হিসেবে সামনে নিয়ে আসতে পারে। কি ধরনের উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থায় ফড়িয়া চরিত্রসম্পন্ন এই ধরনের মহামূর্খ, নীতিবিবর্জিত নিকৃষ্ট ব্যক্তিরা এদেশের সংস্কৃতিক্ষেত্রে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় পাণ্ডা ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে, সে বিষয়ে কোন আলোচনায় যেতে তারা অনিচ্ছুক। এই সমস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা আজ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, মহাপরিচালক প্রভৃতি পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন সেইসব প্রতিষ্ঠানগুলির চরিত্র বিশ্লেষণেও এরা নিতান্তই পরাঙ্মুখ।
এই ব্যক্তিদের সম্পর্কে ব্যক্তিগত পর্যায়ে এইভাবে সমালোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখার মূল কারণ হচ্ছে বর্তমান বাঙলাদেশের প্রায় সমগ্র পেটি-বুর্জোয়া সমাজই আজ এমনভাবে ফড়িয়া চরিত্র লক্ষণসম্পন্ন হয়ে উঠেছে যে এদেশের শিক্ষিত সমাজও (যারা প্রধানতঃ পেটি- বুর্জোয়া) সেই চরিত্র লক্ষণ দ্বারা ভয়ানকভাবে আক্রান্ত। এজন্যেই সমাজের কোন মৌলিক সমালোচনা তারা নিজেরা সাহসিকতার সাথে করতে এগিয়ে আসছে না। সমাজের বিভিন্ন উপসর্গ, অসঙ্গতি, উচ্ছৃঙ্খলতা সম্পের্কে কোন মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করছে না।
শুধু তাই নয়, এরা এ ধরনের সমালোচনার মধ্যে যাচ্ছে না এজন্য যে, পেটি-বুর্জোয়া শিক্ষিত সমাজ বর্তমান নৈরাজ্যের কিছু কিছু টুকরো ফায়দা মাঝে মাঝে পেয়ে যাচ্ছে। শিক্ষিত সমাজের মধ্যে শাসকশ্রেণীর স্বার্থের অনুকূল ‘সংস্কৃতি’ সেবায় কিছুটা যোগ্যতা যাদের আছে তাদের জন্যে বর্তমান শাসক দল অকাতরে অর্থ ব্যয় করছে। তাদের উদ্যোগে সংস্কৃতি সম্মেলন, মহাসম্মেলন, সেমিনার, মেলা অনেক কিছুই হচ্ছে। সংস্কৃতি সেবার নামে যাতে তারা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করতে পারে তার ব্যবস্থা হচ্ছে। যাতে তারা কেউ কেউ বারবার অথবা কেউ কেউ মওকা মতো এক আধবারও বিদেশ যাত্রা করে “ঘরের সংস্কৃতি বাইরে এবং বাইরের সংস্কৃতি ঘরে ছড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ পান তারও ব্যবস্থা হচ্ছে। এইসব ব্যবস্থার ভাগ বাটোয়ারার বখরা লাভের আকাঙ্ক্ষা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা যাদের আছে তারা সমালোচনাকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক করে রাখতেই যে বেশী আগ্রহী হবে তাতে আর সন্দেহ কি? বাঙলাদেশের পেটি-বুর্জোয়া শিক্ষিত সমাজে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সমালোচনার ক্ষেত্রে, এটাই আজ ঘটছে।
এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলেই পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিরা ঐ শ্রেণীরই অন্যান্য অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক অবস্থানে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের যে সমালোচনা করছেন তা সামন্ত সংস্কৃতির ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশের ফলে সৃষ্ট সাংস্কৃতিক নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে চালিত হচ্ছে না। উপরন্তু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তারা সামন্ত সংস্কৃতি ও সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশ সৃষ্ট এই অপসংস্কৃতিরই সেবা করছেন, তাকে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক হচ্ছেন।
১৫
এতো গেল পেটি-বুর্জোয়া শিক্ষিত সম্প্রদায় ও সংস্কৃতিকর্মীদের কথা। তারা যে কোন সমাজে নিজেদের উদ্যোগে সামন্ত সংস্কৃতি ও সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে তাকে তার যথার্থ পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন না তা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। বাঙলাদেশের পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর ওপরে উল্লিখিত বিশেষ কতকগুলি চরিত্র লক্ষণের জন্যে সে কাজ তাদের দ্বারা শ্রেণীগতভাবে আরও অসম্ভব। একাজ তাহলে করবে কারা? ঐতিহাসিকভাবে এ দায়িত্ব কার ওপর বর্তেছে? এর উত্তর হলো : কমিউনিস্টদের ওপর, কমিউনিস্ট পার্টির ওপর। কিন্তু এ দায়িত্ব কি তাদের দ্বারা যথার্থভাবে পালিত হয়েছে অথবা হচ্ছে?
১৬
সামন্ত সংস্কৃতি এবং সংস্কৃতিক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে পাকিস্তানী আমলে ঐক্যবদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি অথবা বিভক্ত কমিউনিস্ট দল-উপদলগুলির সক্রিয়তার যে অভাব ছিলো সে অভাব বাঙলাদেশ-উত্তর পর্যায়ে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই নিষ্ক্রিয়তা এবং ঔদাসীন্য বাঙলাদেশে এমন একটা পরিস্থিতিকে টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করছে যে পরিস্থিতি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষে সহায়ক তো নয়ই, উপরন্তু পর্বতপ্রমাণ এক প্ৰতিবন্ধক।
বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করার পর মাও সেতুঙ ১৯৩৯ সালে লেখা তাঁর ৪ঠা মে আন্দোলন, নামে একটি ছোট প্রবন্ধে বলছেন, ‘কেউ যদি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কেন একজন কমিউনিস্ট প্রথমে একটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সমাজ এবং তারপর সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির চেষ্টা করবে, সেক্ষেত্রে আমাদের জবাব হচ্ছে : আমরা ইতিহাসের অমোঘ গতিপথকেই অনুসরণ করছি।’
কমিউনিস্ট নেতৃত্বে এই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অপর নামই জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব। এই বিপ্লব ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদী ও সাম্রাজ্যবাদ কবলিত দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অনিবার্য পূর্বশর্ত। পৃথিবীর নানা এলাকায় এই ধরনের দেশগুলিতে কিছু কিছু অবস্থার প্রভেদ ও পরিস্থিতির তারতম্য সত্ত্বেও এই অনিবার্য শর্ত সর্বক্ষেত্রেই প্রতিপালিত হতে হবে এবং কমিউনিস্টদেরকে সেই বিপ্লবের পথ শুধু পরিষ্কার করতে হবে তাই নয়, তাতে নেতৃত্ব প্রদান করতে হবে। আমাদের দেশের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য নিশ্চিত করার জন্যে সামন্ত ও সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির ওপর যে আঘাত দরকার এবং যেভাবে দরকার সেটা বাঙলাদেশে তো বটেই এমন কি সারা ভারতীয় উপমহাদেশের কোন এলাকাতেই সম্ভব হয়নি।
কিন্তু তার অর্থ আবার এই নয় যে, ভারতবর্ষ ও বাঙলাদেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি সৃষ্টি ও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে কোন অগ্রগতিই ঘটেনি। তা নিশ্চয়ই ঘটেছে। শিক্ষা সংস্কৃতি শিল্প সাহিত্য ইত্যাদিতে এমন অনেক কিছু নোতুন উপাদান দেখা গেছে যাকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আখ্যা দেওয়া চলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটি কারণে এই ধরনের শিক্ষা সংস্কৃতি শিল্প সাহিত্যচর্চা এদেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের এবং সেই সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথকে সুগম ও ত্বরান্বিত করতে পারেনি।
ওপরে উল্লিখিত প্রবন্ধটিতে চীনে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশের বিভিন্ন স্তর ও পর্যায় সম্পর্কে মাও সেতুঙ বলছেন, ‘অহিফেন যুদ্ধ থেকে শুরু করে বিপ্লবের বিকাশের প্রতিটি পর্যায়েরই কতগুলি পার্থক্য-নির্দেশক বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু তাঁরা কমিউনিস্ট পার্টির আবির্ভাবের পূর্বে এসেছে না পরে এসেছে, এটাই হলো তাদের পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।’
ভারতবর্ষ ও বাঙলাদেশের ক্ষেত্রে কী ঘটেছে? এদেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিকাশ যে একেবারে হয়নি তা নয়। কিন্তু পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যে ‘গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কথা মাও এখানে বলছেন, আমাদের দেশের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিকাশের ক্ষেত্রে সে বৈশিষ্ট্য কি আছে?
আপাতঃদৃষ্টিতে আছে। কারণ এখানে শুধু একটি নয়, অনেকগুলি দলই নিজেদেরকে কমিউনিস্ট হিসেবে অভিহিত করছে এবং এদের প্রত্যেকটিই দাবি করছে যে, তারাই সাচ্চা পার্টি, অন্যেরা জনগণের শ্রেণী শত্রুদের গুপ্তচর মাত্র। কিন্তু কমিউনিস্টদের এই অস্তিত্ব এবং কমিউনিস্ট পার্টি নামে পরিচিত দলসমূহের এই রাজনৈতিক অবস্থান সত্ত্বেও মাও উল্লিখিত ‘গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য’ কি এখানকার বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিকাশের ক্ষেত্রে, সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে?
না, তা মোটেই দেখা যাচ্ছে না। এবং দেখা যাচ্ছে না এজন্যে যে এদেশে কমিউনিস্ট নামে পরিচিত কোন দল বা উপদলই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিকাশের ক্ষেত্রে সহায়ক কতকগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয় কাজ, কতকগুলি অপরিহার্য দায়িত্ব পালন করছে না। শুধু পালন করছে না, বা করতে পারছে না তাই নয়। এ কাজের গুরুত্বই তারা উপলব্ধি করছে না, এ সম্পর্কে তাদের কোন চেতনাই তাদের নীতি, কৌশল ও ক্রিয়াকর্মের মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে না।
ইংরেজ আমলের ভারতবর্ষে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি যখন অবিভক্ত ছিলো তারা গণনাট্য আন্দোলনের মাধ্যমে, গণনাট্য সংঘের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সহায়ক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একটা সংগঠিত প্রচেষ্টা করেছিলো। সেই প্রচেষ্টার ফলে প্রথম দিকে ভারতীয়, বিশেষতঃ বাঙালী সমাজের বিভিন্ন স্তরে একটা আলোড়নও শুরু হয়েছিল। কিন্তু সে আলোড়ন এবং আন্দোলন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশকে তেমন এগিয়ে নিতে পারেনি। কমিউনিস্ট পার্টির অস্তিত্ব মাও-এর বক্তব্য অনুযায়ী যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য পরিস্থিতির মধ্যে সৃষ্টি করার কথা সে পার্থক্য সেখানে সৃষ্টি হয়নি। এই ‘গুরুত্বপূর্ণ’ পার্থক্য সেখানে সৃষ্টি হয়নি, কারণ ভারতবর্ষে তখন যে কমিউনিস্ট পার্টি ছিলো তার মৌলিক চরিত্র ছিলো সংস্কারবাদী ও সংশোধনবাদী। কংগ্রেস-লীগের বুর্জোয়া নেতৃত্বের লেজুড়বৃত্তিই ছিলো তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচির অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। এজন্যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিকাশকে তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে এগিয়ে নিতে পারেনি, উপরন্তু নিজেরাই বুর্জোয়া পেটি বুর্জোয়া ভাবধারার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সংশোধনবাদের জোয়ারে নির্লজ্জভাবে গা ভাসিয়ে দিয়েছে এবং তার ফলেই তাদের গণনাট্য আন্দোলনও পরিশেষে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে মুৎসুদ্দী সংস্কৃতি, সাম্রাজ্যবাদ প্রভাবিত সংস্কৃতিকেই পরিপুষ্ট করেছে।
১৭
পূর্ব পাকিস্তানে এবং বাঙলাদেশে যে গণনাট্য আন্দোলনের মতো কোন আন্দোলনও অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি অথবা বিভক্ত পার্টিগুলির দ্বারা সম্ভব হয়নি সে কথা বলাই বাহুল্য। এবং এ জন্যেই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিকাশের ক্ষেত্রে যে ‘গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যের’ কথা মাও উল্লেখ করেছেন সে পার্থক্য এখানে এখনো পর্যন্ত অনুপস্থিত। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত একের পর এক অনেক আন্দোলনই হয়েছে যেগুলি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষণসম্পন্ন। কিন্তু এই বিপ্লবের বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, তাদের প্রত্যেকটিই পেটি-বুর্জোয়া ভাবধারার দ্বারা মৌলিকভাবে নিয়ন্ত্রিত। এজন্যে তাদের কোনটির মধ্যেই সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের সুষ্ঠু ও শক্তিশালী বিরোধিতা নেই, উপরন্তু আছে তার সাথে আপোষের প্রচেষ্টা। যে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় সামন্তবাদ মূলগতভাবে উচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত কোন দেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হতে পারে না, সেই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় সামন্তবাদের সাথে আপোসের দ্বারাই বাঙলাদেশের মধ্যশ্রেণীর, পেটি-বুর্জোয়াদের বিভিন্ন অংশের সংস্কৃতি আজ পর্যন্ত প্রবলভাবে আচ্ছন্ন ও প্রভাবিত। এই পরিস্থিতিতে এদেশের সংস্কৃতিক্ষেত্রে এবং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিকাশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মাও উল্লিখিত ‘গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যের’ সন্ধান করতে যাওয়া নিতান্তই নিরর্থক।
১৮
কিন্তু ‘ইতিহাসের আমোঘ গতিপথকে অনুসরণ করে’ এদেশের কমিউনিস্টরা সংস্কৃতিক্ষেত্রে এবং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিকাশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই ‘গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য’ সৃষ্টি করতে যতদিন না সক্ষম হবেন ততদিন পর্যন্ত এদেশে যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হবে না সে কথা বলাই বাহুল্য। কাজেই বাঙলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো এই অঞ্চলের কমিউনিস্ট পার্টি ও পার্টিসমূহের ইতিহাসকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করা এবং এ দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বশর্ত কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমস্যাগুলিকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করা এবং সেই সমস্যাগুলোকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আলোকে ও মাও সেতুঙ নির্দেশিত পথ ও পদ্ধতিতে সমাধানের দিকে এগিয়ে নেওয়া।