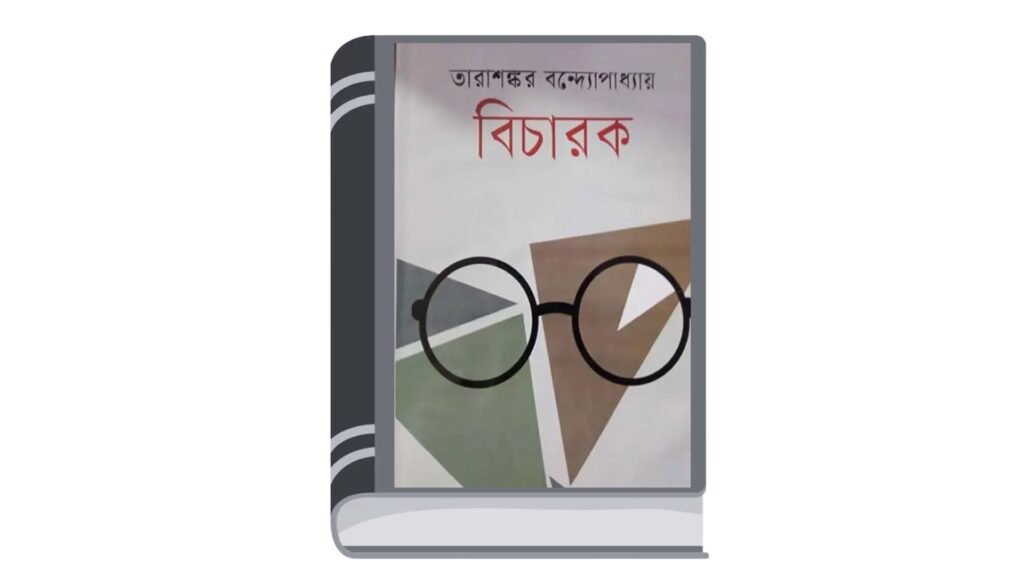০২. ডিভাইন জাস্টিস
ক.
ডিভাইন জাস্টিস!
অবিনাশবাবু কথাটা যেন অভিপ্ৰায়মূলকভাবেই ব্যবহার করেছেন।
কথাটা জ্ঞানবাবু নিজেই বোধ করি অন্যের অপেক্ষা বেশি ব্যবহার করেন। স্কুল প্রমাণ প্রয়োগ যেখানে একমাত্র অবলম্বন, মানুষ যতক্ষণ স্বাৰ্থান্ধতায় মিথ্যা বলতে দ্বিধা করে না, ততক্ষণ ডিভাইন জাস্টিস বোধহয় অসম্ভব। সরল সহজ সভ্যতাবঞ্চিত মানুষ মিথ্যা বললে সে-মিথ্যাকে চেনা যায়, কিন্তু সভ্য-শিক্ষিত মানুষ যখন মিথ্যা বলে তখন সে-মিথ্যা সত্যের চেয়ে প্রখর হয়ে ওঠে। পারার প্রলেপ লাগানো কাচ যখন দর্পণ হয়ে ওঠে তখন তাতে প্রতিবিম্বিত সূর্যটা চোখের দৃষ্টিকে সূর্যের মতই বর্ণান্ধ করে দেয়। জজ, জুরী, সকলকেই প্রতারিত হতে হয়। অসহায়ের মত।
জাস্টিস চ্যাটার্জি বলতেন—He is God, God alone, He can do it.—আমরা পারি না। অমোঘ ন্যায়-বিধানের কর্তব্যবোধ এবং ন্যায়ের মহিমাকে স্মরণে রেখে প্ৰমাণ-প্ৰয়োগগুলি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে, বিন্দুমাত্র ভাবাবেগকে প্রশ্রয় না দিয়ে, আমরা শুধু বিধান অনুযায়ী বিচার করতে পারি।
একটি নারী অপরাধিনীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করার সময় বলেছিলেন তিনি। সুরমা তারই মেয়ে; সুরমা কেঁদে ফেলেছিল—একটা মেয়েকে ফঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেবে বাবা?
চ্যাটার্জি সাহেব বলেছিলেন—অপরাধের ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষের কৃতকর্মের গুরুত্ব এক তিল কমবেশি হয় না মা। দণ্ডের ক্ষেত্রেও নারী বা পুরুষ বলে কোনো ভেদ নাই। ঈশ্বরকে স্মরণ করে এক্ষেত্রে আমার এই দণ্ড না দিয়ে উপায় নেই।
তারই কাছে জ্ঞানেন্দ্রনাথ শিখেছিলেন বিচারের ধারাপদ্ধতি। তিনিই ওঁর গুরু। জ্ঞানেন্দ্রবাবু ঈশ্বর মানেন না। ঈশ্বরকে স্মরণ তিনি করেন না। ঈশ্বর, ভগবান নামটি বড় ভাল। কিন্তু শুধুই নাম। তিনি সাক্ষিও দেন না, বিচারও করেন না, কিন্তু ওই নামের মধ্যে একটা আশ্চর্য পবিত্রতা আছে, বিচারের ক্ষেত্রে একটি আদর্শ আছে; সেটিকেই তিনি স্মরণ করেন। তাই ডিভাইন জাস্টিস। ফিরবার পথে গাড়ির মধ্যে বসে বার বার তিনি আপনার মনে মৃদুস্বরে উচ্চারণ করে। চলেছিলেন–ডিভাইন জাস্টিস ডিভাইন জাস্টিস।
স্থূল প্রমাণ-প্রয়োগের আবরণ ছিঁড়ে মর্ম-সত্যকে আবিষ্কার করে তেমনি বিচার করতে হবে যা অভ্রান্ত, যাকে বলতে পারি ডিভাইন জাস্টিস।
অবিনাশবাবুর কথাগুলি কানের পাশে বাজছে।
ডিভাইন জাস্টিস ডিভাইন জাস্টিস!
স্ত্রী সুরমা দেবী কুঠির হাতার বাগানের মধ্যে বেতের চেয়ার-টেবিল সাজিয়ে বসে বই পড়ছিলেন। সারা দিনের বাদলার পর ঘণ্টাখানেক আগে মেঘ কেটে আকাশ নির্মল হয়েছে, রোদ উঠেছে। সে-রৌদ্রের শোভার তুলনা নেই। ঝলমল করছে সুস্নাত সুশ্যামল পৃথিবী। সম্মুখে। পশ্চিম দিগন্ত অবারিত। কুঠিটা শহরের পশ্চিম প্রান্তে একটা টিলার উপর। এর ওপাশে পশ্চিমদিকে বসতি নেই, মাইল দুয়েক পর্যন্ত অন্য কোনো গ্রাম বা জঙ্গল কিছুই নেই, লাল কাকুরে প্রান্তরের মধ্যে তিন-চারটে অশ্বত্থ গাছ আর একটা তালগাছ বিক্ষিপ্তভাবে এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে আর প্রান্তরটার মাঝখান চিরে চলে গেছে একটা পাহাড়িয়া নদী। ভরা বর্ষায় নদীটা এখন কানায় কানায় ভরে উঠে বয়ে যাচ্ছে। তারই ওপাশ অবধি প্রান্তরের দিগন্তের মাথায় সিঁদুরের মত টকটকে রাঙা অস্তগামী সূর্য। রৌদ্রের লালচে আভা ক্রমশ গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে উঠেছে। গাড়িটা এসে দাঁড়াল। আরদালি নেমে দরজা খুলে দিয়ে সসম্ভ্ৰমে সরে দাঁড়াল। জ্ঞানেন্দ্রবাবু এরই মধ্যে গভীর চিন্তায় ড়ুবে গিয়েছিলেন। স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলেন গাড়ির মধ্যে। আরদালি মৃদুস্বরে ডাকলে হুজুর!
চমক ভাঙল জ্ঞানেন্দ্রবাবুর। ও! বলে তিনি গাড়ি থেকে নামলেন।
সুরমা দেবী স্বামীকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন। বইখানা চায়ের টেবিলের উপর রেখে দিয়ে এগিয়ে এলেন। স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে গাঢ় কণ্ঠেই বললেন– কতদিন চলবে সেস?
একটু হেসে জ্ঞানেন্দ্রনাথ বললেন– বেশিদিন না। সেটা জটিল কিন্তু সাক্ষীর সংখ্যা কম। দিনে বেশি দিন লাগবে না।
বাগানের মধ্যে চায়ের টেবিলটার দিকে তাকিয়ে বললেন– বাগানে চায়ের টেবিল পেতেছ?
সুরমা বললেন–বৃষ্টি আসবে না। দেখছ কেমন রক্তসন্ধ্যা করেছে।
–হ্যাঁ। অপরূপ শোভা হয়েছে। আকাশের দিকে এতক্ষণে তিনি চেয়ে দেখলেন,সুরমা কথাটা বলে দৃষ্টিকে ফিরিয়ে দিতে তবে ফিরল সেদিকে। রক্তসন্ধ্যায় রক্তসন্ধ্যার মধ্যে জীবনের একটি স্মৃতি জড়ানো আছে। সুরমার সঙ্গে যেদিন প্রথম দেখা হয়েছিল, সেদিনও রক্তসন্ধ্যা হয়েছিল আকাশে।
সুরমা বললেন–তাড়াতাড়ি এসে একটু।
–Yes, time and tide wait for none;–হাসলেন জ্ঞানেন্দ্রবাবু।
–শুধু তার জন্যই নয়। কবিতা শোনাব।
–এক্ষুনি আসছি।
জ্ঞানেন্দ্রবাবু হাসলেন। গম্ভীর ক্লান্ত মুখখানি ঈষৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি খুশি হয়ে উঠেছেন। দীর্ঘদিন পর সুরমা কবিতা লিখে তাকে শোনাতে চেয়েছে। সুরমা কবিতা লেখে, তার ছাত্রজীবন থেকেই কবিতা লেখে। তখন লিখত হাসির কবিতা। সেকালে নাম করেছিল। সুরমার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পর তিনিও কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন। কবিতায় সুরমার কবিতার উত্তর দিতেন তিনি। এবং আবিষ্কার করেছিলেন যে তিনিও কবিতা লিখতে পারেন। অন্তত পারতেন। জজিয়তির দপ্তরে তঁর সে-কবিত্ব পাথরচাপা ঘাসের মতই মরে গেছে। কিন্তু সুরমার জীবনে বারমাসে ফুল-ফোটানো গাছের মত কাব্যরুচি এবং কবিকর্ম নিরন্তর ফুটেই চলেছে, ফুটেই চলেছে।
হয়ত অজস্র ফুল ফোটায় সুরমা, কিন্তু সে ফোটে তার দৃষ্টির অন্তরালে তার নিশ্বাসের গণ্ডির বাইরে। কবে থেকে যে এমনটা ঘটেছে তার হিসেব তার মনে নেই, কিন্তু ঘটে গেছে। হঠাৎ একদা আবিষ্কার করেছিলেন যে, সুরমা তাকে আর কবিতা শোনায় না। কিন্তু সে লেখে। প্রশ্ন করেছিলেন সুরমাকে; সুরমা উত্তর দিয়েছিলেন হাসির কবিতা লিখতাম, হাসি ঠাট্টা করেই শোনাতাম। ওসব আর লিখি না। জ্ঞানেন্দ্রনাথ বলেছিলেন যা লেখ তাই শোনাও।
সুরমা বলেছিলেন শোনাবার মত যেদিন হবে সেদিন শোনাব। জ্ঞানেন্দ্রনাথ একটু জোর করেছিলেন, কিন্তু সুরমা বলেছিলেন-ও নিয়ে জোর কোরো না। প্লিজ!
জ্ঞানেন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ পরই ভুলে গিয়েছিলেন কথাটা। বারমাসে ফুল-ফোটানো সেই গাছের মতই সুরমার জীবন-যাতে শুধু ফুলই ফোটে, ফল ধরে না! সুরমা নিঃসন্তান।
আজ সুরমা কবিতা শোনাতে চেয়েছে। চিন্তা-ভারাক্রান্ত মন খানিকটা হালকা হয়ে উঠল। গুরুভারবাহীর ঘর্মাক্ত শ্ৰান্ত দেহে ঠাণ্ডা হাওয়ার খানিকটা স্পর্শ লাগল ফেন।
একবার ভাল করে সুরমার দিকে তাকালেন জ্ঞানেন্দ্রবাবু। পরিণত-যৌবনা এ সুরমার মধ্যে সেই প্রথম দিনের তরুণী সুরমাকে দেখতে পাচ্ছেন যেন। ঘোষাল সাহেব বাঙলোর মধ্যে চলে গেলেন, একটু ত্বরিত পদেই। সুরমা দেবী দাঁড়িয়েই রইলেন পশ্চিম দিগন্তের দিকে চেয়ে।
সুরমার মনেও সেই স্মৃতি গুঞ্জন করে উঠেছে আজ। অনেকক্ষণ থেকে। সাড়ে চারটের সময় বাইরে বারান্দায় এসে দূরের ওই ভরা নদীটার দিকে চেয়ে বসে ছিলেন তিনি। ধীরে ধীরে নিঃশব্দ আয়োজনের মধ্যে আকাশে রক্তসন্ধ্যা জেগে উঠেছিল। তার দৃষ্টি সেদিকে তখন আকৃষ্ট হয় নি। হঠাৎ রেডিওতে একটি গান বেজে উঠল। সেই গানের প্রথম কলি কানে যেতেই আকাশের রক্তসন্ধ্যা যেন মনের দোরে ডাক দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল।
তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর আমার সাধের সাধনা।
শুধু রক্তসন্ধ্যার রর্ণচ্ছটাই নয়, তার সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার স্মৃতিটুকুও বর্ণাঢ্য হয়ে দেখা দিল।
সে কত কালের কথা! বর্ধমানে জজসাহেবের কুঠিতে ছিল তখন তারা। তার বাবা তখন। বর্ধমানে সেসন জজ। উনিশ শো একত্রিশ সাল। আগস্ট মাস। এমনি বর্ষা ছিল সারাদিন। সন্ধ্যার মুখে ক্ষান্তবর্ষণ মেঘে এমনি রক্তসন্ধ্যা জেগে উঠেছিল। বাবা-মা বাড়িতে ছিলেন না, তারা গিয়েছিলেন ইংরেজ পুলিশ সাহেবের কুঠিতে চায়ের নিমন্ত্রণে। নিজে সে তখন কলকাতায় থেকে পড়ত। সেইদিনই সে বাবা-মায়ের কাছে এসেছিল। সেই কারণেই তার নিমন্ত্রণ ছিল না, পুলিশ সাহেব জানতেন না যে সে আসবে। একা বাঙলোর মধ্যে বসে ছিল, হঠাৎ পশ্চিমের জানালার পথে রক্তসন্ধ্যার বর্ণচ্ছটার একটা ঝলক ঘরের মধ্যে এসে পড়েছিল একখানা রঙিন। উত্তরীয়ের মত। এবং গোটা ঘরখানাকেই যেন রঙিন করে দিয়েছিল। একলা বাঙলোর মধ্যে তার যেন একটা নেশা ধরেছিল মনে প্ৰাণে। সে মুক্তকণ্ঠে ওই গানখানি গেয়ে উঠেছিল—
তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর আমার সাধের সাধনা।
****
মম হৃদয়-রক্ত-রঞ্জনে তব চরণ দিয়েছি রাঙিয়া
অয়ি সন্ধ্যাস্বপনবিহারী
মনের উল্লাসে গাইতে গাইতে সে জানালার ধারে এসে দাঁড়িয়েই অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিল। সামনেই বাঙলোর হাতার মধ্যে সিঁড়ির নিচে বাইসিকল ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। সুন্দর, সুপুরুষ, দীর্ঘ-দেহ, গৌরবর্ণ, স্বাস্থ্যবান জ্ঞানেন্দ্রনাথও তখন পূর্ণ যুবক। বেশভূষায় যাকে স্মার্ট বলে তার চেয়েও কিছু বেশি। গলার টাইটি ছিল গাঢ় লাল রঙের, মনে আছে সুরমার। অপ্ৰতিভ হয়ে গান থামিয়ে সরে গিয়েছিল সে জানালার ধার থেকে। এবং আরদালিকে ডেকে প্রশ্ন করেছিল—কে ও? কী চায়?
আরদালি বলেছিল এখানকার থার্ড মন্সব সাহেব। নতুন এসেছে। সাবকে সেলাম দেনে লিয়ে আয়ে থে।
–কতক্ষণ এসেছে? সাহেব নেই বল নি কেন?
–দো মিনিট সে জেয়াদা নেহি। বোলা সাহেব নেহি, চলা যাতে থে, লেকিন বাইস্কিল পাংচার হো গয়া। ওহি লিয়ে দেরি হয়।
বাইসিক্ল পাংচার হয়েছে? হাসি পেয়েছিল সুরমার। বেচারি মুন্সব সাব, এমন সুন্দর স্যুটটি পরে এখন বাইসিক্ল ঠেলতে ঠেলতে চলবেন। বর্ধমানের রাস্তার লাল ধুলো জলে জলে গলে কাদায় পরিণত হয়েছে। মধ্যে মধ্যে খানাখন্দকের ভিতর লাল মিকশ্চার! সুরকি মিকশ্চার! একান্ত কৌতুকভরে সে আবার একবার জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখেছিল।
আজ রেডিওতে ওই গানখানা শুনে রক্তসন্ধ্যার রূপ অপরূপ হয়ে ফুটে উঠেছে সুরমা দেবীর মনে।
খ.
জ্ঞানেন্দ্রনাথ বাঙলোয় ঢুকেই সামনের দেওয়ালের দিকে তাকালেন। ওখানে টাঙানো রয়েছে। তরুণী সুরমার ব্রোমাইড এনলার্জ করা ছবি।
লাবণ্য-ঢলঢল মুখ, মদিরদৃষ্টি দুটি আয়ত চোখ, গলায় মুক্তোর কলারটি সুরমাকে অপরূপ করে তুলেছে। সে-আমলে এত বহুবিচিত্র রঙিন শাড়ির রেওয়াজ ছিল না, পাওয়া যেত না, সুরমার পরনে সাদা জমিতে অল্প-কাজ-করা একখানি ঢাকাই শাড়ি। আর অন্য কোনো রকম শাড়িতে সুরমাকে বোধ করি বেশি সুন্দর দেখাত না। সেদিন জজসাহেবের কুঠিতে দেখেছিলেন শুধু সুরমার মুখ। সিঁড়ির নিচে থেকে তার বেশি দেখতে পান নি। দেখতে চানও নি। রক্তসন্ধ্যার রঙে ঝলমল-করা সে মুখখানার থেকে দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরে নি। দেখবার অবকাশও ছিল না। সুরমা জজসাহেবের মেয়ে; কলেজে পড়েন; প্রগতিশীল সমাজের লোক। জ্ঞানেন্দ্রনাথ তখন মাত্র থার্ড মুনসেফ। গ্রাম্য হিন্দু মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে মাত্র। তার সমাজের লোকে মুনসেফি পাওয়ার জন্য রত্ন বলে, ভাগ্যবান বলে। কিন্তু সুরমাদের সমাজের কাছে নিতান্তই ঝুটো পাথর এবং মুনসেফিকেও নিতান্তই সৌভাগ্যের সান্ত্বনা বলে মনে করেন তারা। সুরমাকে ঠিক এই বেশে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন তাঁর নিজের বাসায়, কিছুদিন পরে। বোধহয় মাস দেড়েক কি দু মাস পর। তাঁর বাসা ছিল শহরের উকিল-মোক্তার পল্লীর প্রান্তে। বেশ একটি পরিচ্ছন্ন খড়ো বাঙলো দেখে বাসাটি নিয়েছিলেন। তখনও ইলেকট্রিক লাইট হয় নি। বাসের জন্য গরমের দেশে খড়ড়া বাঙলোর চেয়ে আরামপ্রদ আর কোনো ঘর হয় না। সামনে একটুকরো বাগানও ছিল। সেদিন কোর্ট শেষ করে বাইসিক্লে চেপে বাড়ির একটু আগে একটা মোড় ফিরে, বাইসিক্লে-চাপা অবস্থাতেই তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁর বাসার দরায় মোটর দাঁড়িয়ে! কার মোটর? পরমুহূর্তে মোটরখানা চিনে তার বিস্ময়ের আর অবধি ছিল না। এ যে সেসন্স্ জজের কার! ওই তো পাশে দাঁড়িয়ে জজসাহেবের আরদালি ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলছে। বাইসিক্ল থেকে বিস্মিত এবং ব্যস্ত হয়ে নেমে আরদালিকে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কে এসেছেন?
আরদালি মুনসেফ সাহেবকে সসম্ভ্ৰমে সেলাম করে বলেছিল-মিস্ সাহেব আমি হ্যায় হুজুর।
মিস্ সাহেব? জজসাহেবের সেই কন্যাটি? সেদিন বাঙলোয় তার গানই শুধু শোনেন নি জ্ঞানেন্দ্রনাথ, তার তীক্ষ্ণ কণ্ঠের আহ্বানও শুনেছিলেন-আরদালি!
শুধু তাই নয়। এই কলেজে পড়া, অতি-আধুনিকা, বাপের আদরিণী কন্যাটি সম্পর্কে ইতিমধ্যে আরও অনেক কথা তিনি শুনেছেন। ব্যঙ্গ-কবিতা লেখে। বাক্যবাণে পারদর্শিনী। এখানকার নিলাম-ইস্তাহার-সর্বস্ব সাপ্তাহিকে জজসাহেবের মেয়ের ব্যঙ্গ-কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। তাও পড়েছেন। আরও একদিন এই মেয়েটিকে দেখেছেন ইতিমধ্যে। সেদিন বাঙলোয় শুধু মুখ দেখেছিলেন; মধ্যে একদিন সব-জজসাহেবের বাড়িতে তার ছোট ছেলের বিয়ে উপলক্ষে প্রীতি-সম্মেলনে মেয়েটিকে জজসাহেবের পাশে বসে থাকতেও দেখেছেন। দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটিকে ভাল লেগেছিল, তেমনি সমও জেগেছিল তার সংযত গাম্ভীর্য দেখে। সেই মেয়ে এসেছেন তার বাড়িতে? কেন? হয়ত প্রগতিশীল রাজকন্যা কোনো সমিতিটমিতির চাঁদার জন্য বা সুমতিকে তার সভ্য করবার জন্য এসে থাকবেন। সুমতি কি–?
আজ সুমতির নাম স্মৃতিপথে উদয় হতেই প্রৌঢ় জ্ঞানেন্দ্রনাথ সুরমার ছবি থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বাঁ দিকের দেওয়ালের দিকে তাকালেন। দেওয়ালটার মাঝখানে কাপড়ের পরদা–ঢাকা একখানা ছবি ঝুলছে।
সুমতির ছবি। সুমতি তার প্রথম পক্ষের স্ত্রী।
একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন জ্ঞানেন্দ্রবাবু। হতভাগিনী সুমতি! জ্ঞানেন্দ্রবাবুর মুখ দিয়ে দুটি আক্ষেপভরা সকাতর ওঃ-ওঃ শব্দ যেন আপনি বেরিয়ে এল। তিনি দ্রুপদে এঘর অতিক্রম করে পোশাকের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।
সুমতির স্মৃতি মর্মান্তিক।
আঃ বলে একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন জ্ঞানেন্দ্রবাবু। মর্মান্তিক মৃত্যু সুমতির। শার্টটা খুলছিলেন তিনি, আঙুলের ডগাটা নিজের পিঠের উপর পড়ল। গেঞ্জিটাও খুলে ফেললেন। পিঠের উপরটার চামড়া অসমতল, বন্ধুর। ঘাড় হেঁট করে বুকের দিকে তাকালেন। বুকের উপরেও একটা ক্ষতচিহ্ন। হাত বুলিয়ে দেখলেন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বুকের ক্ষতচিহ্নটার প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে রইলেন তিনি। বাঁ হাত দিয়ে পিঠের ক্ষতটা অনুভব করছিলেন। গোড়া পিঠটা জুড়ে রয়েছে। ওঃ! এখনও স্পর্শকাতর হয়ে রয়েছে। বিশ বৎসর হয়ে গেল, তবু সারল না। কোট শার্ট গেঞ্জির নিচে ঢাকা থাকে। অতর্কিতে কোনো রকমে চাপ পড়লেই তিনি চমকে ওঠেন। কনকন করে ওঠে। সুমতিকে শেষটায় চিনবার উপায় ছিল না। তিনি শুনেছেন, তবে কল্পনা করতে পারেন। তিনি তখন অজ্ঞান; বোধ করি একবার যেন দেখেছিলেন। বারেকের জন্য জ্ঞান হয়েছিল তার।
পোশাকের ঘরের সঙ্গে সংলগ্ন বাথরুমের ভিতর গিয়ে ঢুকলেন জ্ঞানেন্দ্রবাবু। চৌকির উপর বসে হাতে মুখে জল দিলেন। সাবানদানি থেকে সাবানটা তুলে নিলেন।
ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই সারা বাথরুমটা একটা লালচে আলোর আভায় লাল হয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল; যেন দপ করে জ্বলে উঠেছে কোথাও প্রদীপ্ত আগুনের ছটা! চমকে উঠলেন জ্ঞানেন্দ্রবাবু, হাত থেকে সাবানখানা পড়ে গেল, মুহূর্তের মধ্যে ফিরে তাকালেন পাশের জানালাটার দিকে। ছটাটা ওই দিক থেকেই এসেছে। জানালাটার ঘষা কাচগুলি আগুনের রক্তচ্ছটায় দীপ্যমান হয়ে উঠেছে। একটা নিদারুণ আতঙ্কে তার চোখ দুটি বিস্তারিত হয়ে উঠল, চিৎকার করে উঠলেন তিনি। একটা ভয়ার্ত আর্তনাদ। ভাষা নেই; শুধু রব।
****
দপ করে আগুন জ্বলে উঠেছে বটে কিন্তু অগ্নিকাণ্ড যাকে বলে তা নয়।
জানালাটার ঠিক ওধারেই খানিকটা, বোধ করি আট-দশ ফুট খোলা জায়গার পরই কুঠির বাবুর্চিখানায় বাবুর্চি ওমলেট ভাজছিল। ওমলেট ভাজবার পাত্রটা সম্ভবত মাত্রাতিরিক্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। তার উপর ঘি ঢালতেই সেটা দাউদাউ করে জ্বলে উঠেছে, এবং বিভ্রান্ত পাঁচকের হাত থেকে ঘিয়ের পাত্রটাও পড়ে গেছে। আগুন একটু বেশিই হয়েছিল। তারই ছটা গিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে ঘষা কাচের জানালায়।
তাই দেখেই জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভয়ে বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছেন।
ভয়ার্ত চিৎকার করতে করতে খালি গায়ে, খালি পায়ে ছুটে বেরিয়ে এলেন। সে কী চিৎকার! শুধু ভয়ার্ত একটা ও-ও-ও-শব্দ শুধু। সুরমা দেবী ছুটে এসে তাকে ধরে উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেনকী হল? কী হল! ওগো! ওগো!
থরথর করে কাঁপছিলেন জ্ঞানেন্দ্রবাবু। কিন্তু ধীমান পণ্ডিত ব্যক্তি তিনি, দুরন্ত ভয়ের মধ্যেও তাঁর ধীমত্তা প্ৰাণপণে ঝড়ের সঙ্গে বনস্পতি-শীর্ষের মৃত, লড়াই করে অবনমিত অবস্থা থেকে মাথা তুলে দাঁড়াল। পিছন ফিরে বাঙলোর দিকে তাকালেন তিনি। চোখের ভয়ার্ত দৃষ্টির চেহারা বদলাল, প্রশ্নাতুর হয়ে উঠল। বললেন–আগুন। কিন্তু
অর্থাৎ তিনি খুঁজছিলেন, যে-আগুনকে দাউদাউ শিখায় জ্বলে উঠতে দেখলেন তিনি এক মিনিট আগে—সে আগুন কই? কী হল!
সুরমা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন—আগুন? কোথায়?
আত্মগতভাবেই জ্ঞানেন্দ্রবাবু প্রশ্ন করলেন-কী হল? অগ্নির সে লেলিহান ছটা যে তিনি দেখেছেন, চোখ যে তার বেঁধে গিয়েছে। পরক্ষণেই ডাকলেনবয়।
বয় এসে সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করে বললে—একটুক্ষণ জ্বলেছিল, তারপরই নিতে গিয়েছে।
জ্ঞানবাবু বললেন–এমন অসাবধান কেন? ঘরে আগুন লাগতে পারত!
বয় সবিনয়ে বললে—টিনের চাল–!
–লোকটার নিজের কাপড়চোপড়ে লাগতে পারত। স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন–ওকে জবাব দিয়ে দাও! বলেই হনহন করে বাঙলোর ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন। সুরমা দেবী কোনো উত্তর দিলেন না। স্বামীর পিঠজোড়া ক্ষতচিহ্নের দিকে চেয়ে রইলেন। দীর্ঘদিন পূর্বের কথা তাঁর মনে পড়ল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ এবং সুমতি ঘরে আগুন লেগে জ্বলন্ত চাল চাপা পড়েছিলেন। খবর পেয়ে জজসাহেব এবং সুরমা ছুটে গিয়েছিলেন। ঘরে আগুন লেগেছিল রাত্রে। মফঃস্বল শহরের খড়া বাঙলোবাড়ি, শীতকাল, দরজা-জানালা শক্ত করে বন্ধ ছিল। খড়ের চালের আগুন প্রথম খানিকটা বোধহয় বেশ উত্তাপের আরাম দিয়েছিল। যখন ঘুম ভেঙেছিল সুমতি ও জ্ঞানেন্দ্রনাথের, তখন চারিদিক ধরে উঠেছে। দরজা খুলে বের হতে হতে সামনের চালটা খসে নিচে পড়ে যায়। সুমতি, জ্ঞানেন্দ্রবাবু জ্বলন্ত চাল চাপা পড়েন। জ্ঞানেন্দ্রবাবু তার হাত ধরে বের করে আনছিলেন; মাঝখানে সুমতি কাচে পা কেটে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। জ্ঞানেন্দ্রনাথও ছিটকে সামনে পড়ে বুকে পিঠে জ্বলন্ত খড় চাপা পড়েন। সুমতির সর্বাঙ্গ পুড়ে ঝলসে গিয়েছিল। ওঃ, সে কী মর্মান্তিক দৃশ্য! জ্ঞানেন্দ্রনাথ তখন হাসপাতালের ভিতরে বেডের উপর অজ্ঞান অবস্থায় শুয়ে। সুমতির দেহটা কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল। তুলে দেখিয়েছিল ডাক্তার।
ওঃ! ওঃ! ওঃ! সুরমা দেবীও চোখ বুজে শিউরে উঠলেন।
গ.
কী মিষ্টি চেহারা কী বীভৎস হয়ে গিয়েছিল! উঃ! সুমতিকে মনে পড়ছে। শ্যাম বৰ্ণ, একপিঠ কালো চুল, বড় বড় দুটি চোখ, একটু মোটাসোটা নরম-নরম গড়ন; মুক্তোর পতির মত সুন্দর দাঁতগুলি, হাসলে সুমতির গালে টোল পড়ত। এবং দুজনের মধ্যে অনির্বচনীয় ভালবাসা ছিল। অফিসার মহলে এ নিয়ে কত জল্পনা-কল্পনা হয়েছে। হওয়ারই কথা। ব্রাহ্ম বিলেতফেরত ব্যারিস্টার জজসাহেবের কলেজে-পড়া মেয়ের সামান্য মুনসেফের স্ত্রী গ্রাম্য জমিদার-কন্যা অর্ধশিক্ষিতা সুমতির সঙ্গে এত নিবিড় অন্তরঙ্গতা কিসের? কেউ বলেছিল—কোথায় কোন জেলা স্কুলে সুরমা ও সুমতি একসঙ্গে পড়ত। কেউ বলেছিল সুরমা ও সুমতির পিতৃপক্ষ কোনকালে দার্জিলিং গিয়ে পাশাপাশি ছিলেন, তখন থেকে সখী দুজনে। হঠাৎ এখানে সবজজের বাড়িতে দুজনে দুজনকে চিনে ফেলে, পুরনো সখিত্ব নতুন করে গড়ে তুলছে। কিন্তু সবকিছুর মধ্যেই একটানা-একটা অসঙ্গতি বেরিয়েছেই বেরিয়েছে। শেষ পর্যন্ত সত্য কথাটা প্রকাশ পেল।
সুমতি ছিল তার নিজের পিসতুতো বোন; জজসাহেব অরবিন্দ চ্যাটার্জি সুমতির মামা। সুমতির মায়ের সহোদর ভাই। কলেজে পড়বার সময় ব্রাহ্ম হয়ে সুরমার মাকে বিবাহ করেছিলেন। বাপ ত্যাজ্যপুত্র করেন। ছেলের নাম মুখে আনতে বাড়িতে বারণ ছিল। কোনো সম্পর্কও ছিল না দুই পক্ষের মধ্যে। অরবিন্দবাবু বিলেত গেলেন, ব্যারিস্টার হয়ে এসে বিচার বিভাগে চাকরি নিয়ে সম্পূর্ণরূপে আলাদা মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর পক্ষে খবর না রাখাই স্বাভাবিক। পিতৃপক্ষও রাখতেন না। রাখেন নি। বরং এই ছেলের নাম তারা সযত্নে মুছে দিয়েছিলেন সেকালের সামাজিক কলঙ্ক ও লজ্জার বিচিত্র কারণে। এ-পরিচয় প্রকাশ হলে সেকালে সামাজিক আদান-প্ৰদান কঠিন হয়ে পড়ত। সুমতি তার মায়ের কাছে মামার নাম শুনেছিল। শুনেছিল, তিনি ব্রাহ্ম হয়ে বাড়ি থেকে চলে গেছেন, এই পর্যন্ত। তার মা বিয়ের সময় বার বার করে বলে দিয়েছিলেন, মামার কথা যেন গল্প করিস নে। কী জানি কে কীভাবে নেবে। সুরমা অবশ্য গল্প শুনেছিল, তার বাবার কাছে। ইদানীং জজসাহেব অরবিন্দ চ্যাটার্জি একটু ভাবপ্রবণ হয়ে উঠেছিলেন। বিশেষ করে রাত্রিকালে ব্র্যান্ডি পান করে মায়ের জন্য কাঁদতেন। বলতেন, মাই মাদার ওয়াজ এ গডেস! আর কী সুন্দর তিনি ছিলেন। সাক্ষাৎ মাতৃদেবতা! যেন সাক্ষাৎ আমার বাংলাদেশ! শ্যামবর্ণ, একপিঠ ঘন কালো চুল, বড় বড় চোখ, মুখে মিষ্টি হাসি, নরম-নরম গড়ন—আহা-হা!
সুমতির চেহারা ছিল ঠিক তার মত, নিজের মায়ের মত। সেই দেখেই প্রকাশ পেল সেই পরিচয়। চিনলেন চ্যাটার্জি সাহেব নিজেই। বর্ধমানে সুমতিরা মাসদুয়েক এসেছে তখন। সবজজের বাড়িতে ছোট ছেলের বিবাহে সামাজিক অনুষ্ঠান-বউভাতের প্রীতিভোজন। সুরমা, সুরমার মা এবং বাবা বাইরের আসরে বসে ছিলেন, সেখানে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, পুলিশ সাহেব, ডাক্তার সাহেবরাও সস্ত্রীক বসে ছিলেন, পাশে একটু তফাত রেখে বসেছিলেন ডেপুটি, সবডেপুটি, মুনসেফের দল। তাদের গৃহিণীদের আসর হয়েছিল ভিতরে; এই আসরের মাঝখানের পথ দিয়েই তারা ভিতরে যাচ্ছিলেন। সুমতিও চলে গিয়েছিল। সুরমার বাবা কথা বলছিলেন ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে। তিনি অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলেন, দৃষ্টিতে ফুটে উঠল অপরিসীম বিস্ময়। পরক্ষণেই অবশ্য তিনি আত্মসংবরণ করে আবার কথা বলতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু সেই ক্ষণিকের বিস্ময়-বিমূঢ়তা লক্ষ্য করেছিলেন অনেকেই। সুরমার মারও চোখ এড়ায় নি। কিছুক্ষণ পর যে কথা তিনি বলছিলেন সেই কথাটা শেষ হতেই আবার যেন গভীর অন্যমনস্কতায় ড়ুবে গেলেন। সুরমার মা আর আত্মসংবরণ করতে পারেন নি, মৃদুস্বরে প্রশ্ন করেছিলেন-কী ব্যাপার বল তো?
—অ্যাঁ—? চমকে উঠেছিলেন সুরমার বাবা।
স্ত্রী জিজ্ঞাসা করেছিলেন—হঠাৎ কী হল তোমার? তখন এমনভাবে চমকে উঠলে? আবারও যেন কেমন তন্ময় হয়ে ভাবছ!
–কতকাল পর হঠাৎ যেন মাকে দেখলাম। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চ্যাটার্জি সাহেব কথাটা বলেছিলেন।–অবিকল আমার মা। অবিকল! তফাত, এ মেয়েটি একটু মডার্ন।
—কে? কী বলছ তুমি?
–লালপেড়ে গরদের শাড়ি পরে একটি মেয়ে তখন বাড়ির ভিতর গেল, দেখেছ? শ্যামবর্ণ, বড় বড় চোখ, কপালে সিঁদুরের টিপটা একটু বড়, গোঁড়া হিন্দুর ঘরে যেমন পরে। অবিকল আমার মা! ছেলেবেলায় যেমন দেখতাম।
এর উত্তরে সুরমার মা কী বলবেন, চুপ করেই ছিলেন। চ্যাটার্জি সাহেবও কয়েক মিনিটের জন্য চুপ করে গিয়েছিলেন। তারপর হঠাৎ একটু সামনে ঝুঁকে মৃদুস্বরে বলেছিলেন—একটু খোঁজ নিতে পার? কে, কে এ মেয়েটি? সহজেই বের করতে পারবে, লালপেড়ে গরদের শাড়ি পরে এসেছে, ভারি নরম চেহারা, কচি পাতার মত শ্যামবর্ণ, বড় বড় চোখ, কপালে সিঁদুরের টিপটা বড়। সহজেই চেনা যাবে। দেখ না? দেখবে?
অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেন নি সুরমার মা। এবং সহজেই সুমতিকে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। ফিরে এসে বলেছিলেন—এখানে নতুন মুনসেফ এসেছেন, মিস্টার ঘোষাল, তাঁর স্ত্রী।
—থার্ড মুনসেফের স্ত্রী? একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন, অবিকল আমার মা। মেয়েটির সিঁথির ঠিক মুখে, এই আমার এই কপালে যেমন একটা চুলের ঘূর্ণি আছে, তেমনি একটা ঘূর্ণি আছে। আমার মায়ের ছিল।
সেদিন রাত্রে বাড়ি ফিরে চ্যাটার্জি সাহেব মদ্যপান করে মায়ের জন্য হাউহাউ করে কেঁদেছিলেন। নিশ্চয় আমার মা! এ জন্মে
সুরমার মা বলেছিলেন পুনর্জন্মঃ বোলা না, লোকে শুনলে হাসবে।
হঠাৎ চ্যাটার্জি সাহেব বলেছিলেন তা না হলে এমন মিল কী করে হল? ইয়েস। হতে পারে। সুরো, মামি, তুমি একবার কাল যাবে এই মেয়ের কাছে? তুমি স্বচ্ছন্দে যেতে পার। জেনে। এসো, ওর বাপের নাম কী, ঠাকুরদাদার নাম কী, কোথায় বাড়ি?
সুরমার মার খুব মত ছিল না, কিন্তু প্রৌঢ় বাপের এই ছেলেমানুষের মত মা-মা করা দেখে সুরমা বেদনা অনুভব করেছিল, না-গিয়ে পারে নি।
সুমতি অবাক এবং সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল প্রথমটা। খোদ জজসাহেবের মেয়ে এসেছেন, কলেজ-পড়া আধুনিকা মেয়ে! যে-মেয়ে সমাজে সভায় তাদের থেকে অনেক তফাতে এবং উঁচুতে বসে, সে নিজে এসেছে তাদের বাড়ি।
সুরমা গোপন করে নি। সে হেসে বলেছিল—আপনি নাকি অবিকল আমার ঠাকুরমার মত দেখতে। এমনকি আপনার সিঁথির সামনের চুলের এই ঘূর্ণিটা পর্যন্ত। আমার বাবার মধ্যে আবার একটি ইন্টারন্যাল চাইল্ড, মানে চিরন্তন খোকা আছে। মায়ের নাম করে প্রায় কদেন। কাল সে কী হাউহাউ করে কান্না। তাই এসেছি, আপনার সঙ্গে ঠাকুমা পাতাতে।
সুমতি স্থির দৃষ্টিতে সুরমার দিকে তাকিয়ে ছিল কিছুক্ষণ।
সুরমা হেসে বলেছিল—অবাক হচ্ছেন? অবাক হবার কথাই বটে। কিন্তু আপনার বাপের বাড়ি কোথায়, বলুন তো? আপনি কি অবিকল আপনার ঠাকুরমার মত দেখতে?
সুমতি বলেছিল–না। তবে আমার দিদিমার সঙ্গে আমার চেহারার খুব মিল। মা বলেন–অবিকল।
এর উত্তরে আসল সম্পর্ক আবিষ্কৃত হতে বিলম্ব হয় নি। সুমতি ছিল অবিকল তার দিদিমার মত দেখতে। দিদিমা তার জন্মের পরও কয়েক বছর বেঁচে ছিলেন, নইলে এই ঘটনার পর অন্তত লোকে বলত, তিনিই ফিরে এসে সুমতি হয়ে জন্মেছেন, এবং ধর্মান্তরগ্রহণ-করা অরবিন্দ চ্যাটার্জি জজসাহেবের সঙ্গে এই দেখা হওয়াটি একটি বিচিত্র ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাত হত; লোকে বলত জজসাহেব-ছেলের সমাদর পাবার জন্যই ফিরে এসেছেন তিনি। এসব কথা সুমতি বলে নি, বলেছিল সুরমা। সুমতি খুব হেসেছিল, খুব হাসতে পারত সে। ঠিক এই সময়েই বাসার বাইরে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। দরজায় জজসাহেবের আরদালি এবং গাড়ি দেখে কী করা উচিত ভেবে না পেয়ে সেইখানেই দাঁড়িয়ে ছিলেন নিজ বাসভূমে পরবাসীর মত। সারাটা দিন মুনসেফ কোর্টে রেন্ট-সুট আর মনি-সুটের জট ছাড়িয়ে, কলম পিষে, শ্ৰান্ত দেহ ও ক্লান্ত মস্তিষ্ক নিয়ে মাইল তিনেক বাইসিক্ল ঠেঙিয়ে বাড়ি ফিরে দেখেছিলেন গৃহদ্বার একরকম রুদ্ধ, খোলা থাকলেও প্রবেশাধিকার নেই। বাইরের ঘরে সুমতির সঙ্গে কথা বলতে বলতে সুরমাই জ্ঞানেন্দ্রনাথের এই ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা দেখতে পেয়েছিল এবং প্রচুর কৌতুকে বয়স-ও স্বভাব-ধর্মে কৌতুকময়ী হয়ে উঠেছিল।
ঘ.
বয়!
সুরমা চমকে উঠলেন। স্বামী বাঙলোর মধ্যে ফিরে যাওয়ার পর থেকেই সুরমা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েই ছিলেন। স্বামীর ভয়ার্ত অবস্থা এবং পিঠের বুকের ক্ষতচিহ্ন দেখে অতীত কথাগুলি মনে পড়ে গিয়েছিল। সুমতির ওই মর্মান্তিক মৃত্যুস্মৃতির বেদনার মধ্যে তাঁর নিজের তরুণ জীবনের পূর্বরাগের রঙিন দিনগুলির প্রতিচ্ছবি ফুটে রয়েছে। একরাশি কালে কয়লার উপর কয়েকটি মরা প্রজাপতির মত।
স্বামীর কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলেন তিনি। পাজামা, পাঞ্জাবি পরে রবারের স্লিপার পায়ে কখন যে উনি এসেছেন তা তিনি জানতে পারেন নি। বাঙলোর দিকে পিছন ফিরে রক্তসন্ধ্যার দিকেই তিনি তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।
জ্ঞানেন্দ্রনাথ চেয়ার টেনে বসে পড়লেন, তাঁর চোখ-মুখ এখনও যেন কেমন থমথম করছে। তাকে দেখে সুরমা শঙ্কিত হলেন, মনে হল ক্লান্ত বড় তিনি। সুরমা এগিয়ে এসে মিঃ ঘোষালের পিছন দিকে দাঁড়িয়ে তার কাঁধের উপর নিজের হাত দুখানি গাঢ় স্নেহের সঙ্গে রেখে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন ডাক্তারকে একবার খবর দেব?
—ডাক্তার? একটু চকিত হয়ে উঠলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ–কেন?
—তুমি অত্যন্ত আপসেট হয়ে গেছ। নিজে বোধহয় ঠিক বুঝতে পারছ না। এখনও পর্যন্ত
পিছন দিকে হাত বাড়িয়ে স্ত্রীর হাতখানি ধরে জ্ঞানেন্দ্রবাবু বললেন– না। ঠিক আছি আমি।
–না। তুমি তোমার আজকের অবস্থা ঠিক বুঝতে পারছ না। আগুন নিয়ে তোমার ভয় আছে। একটুতেই চমকে ওঠ, কিন্তু এমন তো হয় না। তোমার বিশ্রাম নেওয়া উচিত। আর এভাবে পরিশ্রম–
বাধা দিয়ে জ্ঞানেন্দ্রনাথ হেসে বললেন–নাঃ, আমি ঠিক আছি। আজকের ঘটনাটা একটু অস্বাভাবিক।
—আগুনটা কি খুব বেশি জ্বলে উঠেছিল?
—উঃ, সে তুমি কল্পনা করতে পারবে না। বাথরুমের জানালার কাচের মধ্যে দিয়ে রিফ্লেকশ্যনে ঘরটা একেবারে রাঙা হয়ে উঠেছিল! অবশ্য আমিও একটু-একটু, কী বলব, dreamy, স্বধাতুর ছিলাম। ঠিক শক্তমাটির উপর দাঁড়িয়ে ছিলাম না। চমকে একটু বেশি উঠেছি।
–মানে?
–বলছি। সামনে এস, পিছনে থাকলে কি কথা বলা হয়?
সুরমা সামনের চেয়ারে এসে বসলেন। এঁদের দুজনের পিছনে বাবুর্চি চায়ের ট্রে এবং খাবার নিয়ে অপেক্ষা করছিল, সাহেব এবং মেমসাহেবের এই হাত-ধরাধরি অবস্থার মধ্যে সামনে আসতে পারছিল না, সে এইবার সুযোগ পেয়ে এগিয়ে এসে টেবিলের উপর চায়ের সরঞ্জামগুলি নামিয়ে দিল।
সুরমা বললেন–যাও তুমি, আমি ঠিক করে নিচ্ছি সব।
জ্ঞানেন্দ্রনাথ বললেন–ইয়ে দুফে তুমহারা কসুর মাফ কিয়া গয়া, লেকিন দুসরা দফে নেহি হোগা। হুঁশিয়ার হোনা চাহিয়ে। তুমহারা সুগামে আগ লাগা যাতা তো কেয়া হোতা? আঁঃ?
সেলাম করে বাবুর্চি চলে গেল।
জ্ঞানেন্দ্রনাথ বললেন–আজকের ঘটনাগুলো আগাগোড়াই আমাকে একটুকী বলব–একটু ভাবপ্রবণ করে তুলেছিল। এখানে এসেই তোমাকে দেখলাম, রক্তসন্ধ্যার আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছ। সেই পুরনো কবি-কবি ভাব! দীর্ঘদিন পর বললে কবিতা শোনাব। পুরনো শুকনো মাটিতে নতুন বর্ষার জল পড়লে সেও খানিকটা সরস হয়ে ওঠে। আমার মনটাও ঠিক তা-ই হয়ে উঠেছিল। মনে পড়ে গেল একসঙ্গে অনেক কথা। রক্তসন্ধ্যার দিন বর্ধমান জজকুঠিতে তোমাকে দেখার কথা। ঘরে ঢুকেই ওদিকের দরজার মাথায় তোমার সেই ছবিটা দ্যাট রিমাইন্ডেড মিসেই প্রথম দিনের পরিচয় হওয়ার কথা মনে পড়িয়ে দিলে। স্বাভাবিকভাবে মনে পড়ল সুমতিকে। সেই হতভাগিনীর কথা ভাবতে ভাবতেই বাথরুমে ঢুকেছিলাম। গেঞ্জি খুলতে গিয়ে রোজই পিঠের পোড়া চামড়ায় হাত পড়ে। আজও পড়েছিল। কিন্তু আজ মনে পড়ছিল সেই আগুনের কথা। ঠিক মনের এই ভাববিহ্বল অবস্থার মধ্যে হঠাৎ বাইরে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। আমার মনে হল আমাকে ঘিরে আগুনটা জ্বলে উঠল।
চায়ের কাপ এবং খাবারের প্লেট এগিয়ে দিলেন সুরমা। মৃদুস্বরে বললেন–তবু বলব আজ ব্যাপারটা যেন কেমন। আগুনকে ভয় তোমার স্বাভাবিক। কিন্তু
আগুনকে ভয় তাঁর স্বাভাবিক, অতর্কিত আগুন দেখলে চকিত হয়ে ওঠেন, খড়ের ঘরে শুতে পারেন না, রাত্রে বালিশের তলায় দেশলাই পর্যন্ত রাখেন না। সিগারেট পর্যন্ত খান না তিনি। বাড়ির মধ্যে পেট্রোল-কেরোসিনের টিন রাখেন না। কখনও খোলা জায়গায় ফায়ারওয়ার্ক দেখতে যান না। কিন্তু আজ যেন ভয়ে কেমন হয়ে গিয়েছিলেন তিনি।
চায়ের কাপে চামচ নাড়তে নাড়তে হেসে জ্ঞানেন্দ্রবাবু বোধ করি সমস্ত ঘটনাকে হালকা করে দেবার অভিপ্ৰায়েই হেসে সুরমার দিকে তৰ্জনী বাড়িয়ে দেখিয়ে বললেন–সব কিছু না। তুমি! সমস্তটার জন্য রেসপন্সিবল তুমি।
—আমি?
–হ্যাঁ, তুমি। কবি হলে বলতাম, এলোচুলে বহে এনেছ কি মোহে সেদিনের পরিমল! বললাম তো—আজকের তোমাকে দেখে প্রথম দিনের দেখা তোমাকে মনে পড়ে গেল। এবং সব গোলমাল করে দিলে! জজসাহেবের কলেজে-পড়া তরুণী মেয়েটি সেদিন যেমন মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল, আজও মাথাটা সেইরকম ঘুরে গেল!
হেসে ফেললেন সুরমা দেবী।
জ্ঞানেন্দ্রবাবু বললেন–ওঃ সেদিন যা সম্বোধনটা করেছিলে! ভ্যাবাকান্ত।
এবার সশব্দে হেসে উঠলেন সুরমা। বললেন–বলবে না? নিজের বাড়ির দোরে এসে বাড়িতে জজসাহেবের কলেজে-পড়া মেয়ে এসেছে শুনে একজন মডার্ন তরুণ যুবক পেটজ্বালা-করা ক্ষিদে নিয়ে মুখ চুন করে ফিরে যাচ্ছেন। কী বলতে হয় এতে তুমি বল না? গাইয়া। কোথাকার!
সেদিন বাড়ির দোর থেকে মুখ চুন করে সত্যিই ফিরে যাচ্ছিলেন থার্ড মুনসেফ জ্ঞানেন্দ্রনাথ। কী করবেন? জজসাহেবের কলেজে-পড়া মেয়ে, কোথায় কী খুঁত ধরে মেজাজ খারাপ করবে, কে জানে। তার চেয়ে ফিরে যাওয়াই ভাল। ঠিক এই সময়েই সামনের ঘরের পরদা সরিয়ে সুরমাই আবির্ভূত হয়েছিল; জ্ঞানেন্দ্রনাথের বিব্রত অবস্থা দেখে অন্তরে অন্তরে কৌতুক তার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। সেদিন তখন সে জজসাহেবের মেয়ে এবং জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুনসেফ নয়; আত্মীয়তার মাধুর্য, পদমর্যাদার পার্থক্যের রূঢ় ভুলিয়ে দিয়েছে, বরং খানিকটা মোহের সৃষ্টি করেছিল এমন বিচিত্র ক্ষেত্রে। তাই সুমতির আগে সে-ই পরদা সরিয়ে মৃদু হেসে। বলেছিল—আসুন মিস্টার ঘোষাল; বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন যে! আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছি। আলাপ করতে এসেছি।
সুমতি সুরমার পাশ দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হেসে বলেছিল—এস। সুরমা আমার মামাতো বোন। ওর বাবা আমার সেই মামা, যিনি বাড়ি থেকে চলে গিয়ে–
বাকিটা উহ্যই রেখেছিল সুমতি।
—কী আশ্চর্য!
একমাত্র ওই কথাটিই সেদিন খুঁজে পেয়েছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ।
সুরমা বলেছিল-টুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশ্যন।
জ্ঞানেন্দ্রনাথ কিন্তু তখনও বসেন নি। বসতে সাহসই বোধ করি হয় নি অথবা অবস্থাটা ঠিক স্বাভাবিক বলে বিশ্বাস হচ্ছিল না। সুরমাই বলেছিল কিন্তু আপনি বসুন। দাঁড়িয়ে রইলেন যে? আমি তো আপনাদের আত্মীয়া। আপনজন!
বেশ ভঙ্গি করে একটু ঘাড় দুলিয়ে চোখ দুটি বড় করে বক্ৰ হেসে সুমতি বলেছিল—অতিমিষ্টি আপনজন, শালী।
সুরমাতে গ্রাম্যতার ছোঁয়াচ লেগে গিয়েছিল মুহূর্তে। সভ্যতাকে বজায় রেখে জ্ঞানেন্দ্রনাথের মত সুপুরুষ অপ্রতিভ বিব্রত তরুণটিকে বিদ্রুপ না করে তৃপ্তি হচ্ছিল না। এই গ্রাম্য ছোঁয়াচের সুযোগ নিয়ে উচ্ছল হয়ে সে বলে উঠেছিলহলে কী হবে, ভগ্নীপতিটি আমার একেবারে ভ্যাবাকান্ত।
সুমতি হেসে উঠেছিল।
পরক্ষণেই নিজেকে সংশোধন করবার অভিপ্ৰায়েই সুরমা বলেছিল মাফ করবেন। রাগ করবেন না যেন।
সুমতি আবারও তেমনি ধারায় ঘাড় দুলিয়ে বলেছিলশালীতে ওর চেয়েও খারাপ ঠাট্টা করে। এ আবার লেখাপড়া-জানা আধুনিকা শালী; এ ঠাট্টা ভেঁাতা নয়, চোখা।
এতক্ষণে জ্ঞানেন্দ্রনাথ একটা ভাল কথা খুঁজে পেয়েছিলেন, বলেছিলেন শ্যালিকার ঠাট্টা খারাপ হলেও খারাপ লাগে না, চোখা হলেও গায়ে বেঁধে না। মহাভারতে অর্জুনের প্রণাম-বাণ। চুম্বন-বাণের কথা পড়েছ তো? বাণ–একেবারে শানানো ঝকঝকে লোহার ফলা-বসানো তীর-সে-তীর এসে পায়ে লুটিয়ে পড়ত, কিংবা কপালে এসে মিষ্টি ছোঁয়া দিয়ে পড়ে যেত। শ্যালিকার ঠাট্টা তাই। ওদের কথাগুলো অন্যের কাছে শানানো বিষানো মনে হলেও ভগ্নীপতিদের কানের কাছে পুষ্পবাণ হয়ে ওঠে। তার উপর ওঁর মত শ্যালিকা।
সুমতি চা করতে করতে মুহূর্তে মাথা তুলে তাদের দিকে তাকিয়েছিল। কুঞ্চিত দুটি জ্বর নিচে সে-দৃষ্টি ছিল তীব্র এবং তীক্ষ্ণ। বলেছিল—কী কথার শ্রী তোমার! ও তোমাকে পুষ্পবাণ মারতে যাবে কেন? পুষ্পবাণ কাকে বলে? কী মনে করবে সুরমা?
জ্ঞানেন্দ্রনাথ সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছিলেন, ঘরের পরিমণ্ডল অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছিল।
ঙ.
কথাটা দুজনেরই মনে পড়ে গেল। অতীত কথার সরস স্মৃতি স্মরণ করে যে-আনন্দমুখর সন্ধ্যার আকাশে তারা ফোটার মত ফুটে ফুটে উঠছিল, তার উপর একখানা মেঘ নেমে এল। দুজনেই প্রায় একসঙ্গে চুপ করে গেলেন। একটু পর সুরমা দেবী জিজ্ঞাসা করলেন আর একটু চা নেবে না?
–না।
স্থিরদৃষ্টিতে দিগন্তের দিকে চেয়ে ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। না বলেই তিনি উঠে পড়লেন চেয়ার থেকে। পিছনের দিকে হাত দুটি মুড়ে পায়চারি করতে লাগলেন। হাতার ওপাশে একটা রাখাল একটা গরুকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ওঃ! সুমতি তাকে ওর চেয়েও নিষ্ঠুর তাড়নায় তাড়িত করেছে। ওঃ! গরু-মহিষের দালালরা ডগায় উঁচ বা আলপিন-গোঁজা লাঠির খোঁচায় যেমন করে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায় তেমনিভাবে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। সে কী নিষ্ঠুর যন্ত্রণা! যে-যন্ত্রণায় জীবনের সমস্ত বিশ্বাস তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন ঈশ্বরে বিশ্বাস, ধর্মে বিশ্বাস, সব বিশ্বাস। ঈশ্বরের নামে শপথ করেছেন তিনি সুমতির কাছে, ধর্মের নামে শপথ করেছেন। সুমতি মানে নি। দিনের মাথায় দু-তিন বার বলত বল, ভগবানের দিব্যি করে বল! বল, ধর্মের মুখ চেয়ে বল!
তিনি বলেছেন। তার শপথ নিয়ে বললে বলেছে—আমি মরলে তোমার কী আসে যায়? সে তো ভালই হবে!
ওই প্রথম দিন থেকেই সন্দেহ করেছিল সুমতি। সে বার বার বলেছে—ওইওই এক কথাতেই আমি বুঝেছিলাম। সে-ই প্রথম দিন। তার চোখ দুটো জ্বলন্ত। প্রথম দিন রহস্যের আবরণ দিয়ে যে কথাগুলি বলেছিল তার প্রতিটির মধ্যে এ সন্দেহের আভাস ছিল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ সুরমা দুজনের একজনও সেটা ধরতে পারেন নি সেদিন।
অরবিন্দ চ্যাটার্জির মত উদার লোককেও সে কটু কথা বলত। নিজের মায়ের সঙ্গে নিবিড় সাদৃশ্যের জন্য চ্যাটার্জি সাহেবের স্নেহের আর পরিসীমা ছিল না। সুমতিকে দিয়েথুয়ে তার আর আশ মিটত না। সুমতির স্বামী বলে জ্ঞানেন্দ্রনাথের ওপরেও ছিল তার গভীর স্নেহ। সে-স্নেহ তাঁর গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়েছিল জ্ঞানেন্দ্রনাথের বুদ্ধিদীপ্ত অন্তরের স্পর্শে, জ্ঞানেন্দ্রনাথের উদার মন এবং প্রসন্ন মুখশ্রীর আকর্ষণে। তিনি ওঁকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। সুমতি তার কাছে ঘেঁষতে চাইত না; অরবিন্দুবাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথকে কাছে টেনে ওঁরই হাত দিয়ে সুমতিকে স্নেহের অজস্র সম্ভার পাঠাতে চাইতেন। ওঁর জীবনের উন্নতির পথ তিনিই করে দিয়েছিলেন। রায় লেখার পদ্ধতি, বিচারের সিদ্ধান্তে উপনীত হবার কৌশল—তিনিই ওঁকে শিখিয়েছিলেন। এসব কিছুই কিন্তু সহ্য হত না সুমতির। তাঁর পাঠানো কোনো জিনিস জ্ঞানেন্দ্রনাথ নিয়ে এলে তা ফেরত অবশ্য পাঠাত না সুমতি, কিন্তু তা নিজে হাতে গ্রহণ করত না। বলত—এইখানে রেখে দাও। কী বলব দেওয়াকে। আর কী বলব দিদিমার চেহারার সঙ্গে আমার আদকে। কী বলব জজসাহেবের বুড়ো বয়সে উথলে-ওঠা ভক্তিকে। গরু মেরে জুতো দান! সেই দান আমার নিতে হচ্ছে।
রায় লেখা বা বিচার-পদ্ধতি শেখানো নিয়ে বলত—মুখে ছাই বিচার-শেখানোর মুখে। যে একটা মেয়ের জন্যে ধর্ম ছাড়তে পারে, সে তো অধার্মিক। যে অধার্মিক, সে বিচার করবে কী? ধর্ম নইলে বিচার হয়? আর সেই লোকের কাছে বিচার শেখা!
থাক। সুমতির কথা থাক! সুমতির ছবি দেওয়ালে টাঙানো থেকেও পরদাঢকা থাকে। অরবিন্দবাবু বলতেন, সুমতির কথা নিয়ে বলতেন—কী করবে? সহ্য কর। ভালবাস ওকে। Love is God, God is Love.
চ্যাটার্জিসাহেব বলতেন ঈশ্বরের অস্তিত্বে আমি বিশ্বাস করি নে। ব্ৰহ্ম-ব্ৰহ্ম ওসবও না। আমি একটি মেয়েকে ভালবেসেছিলাম, সে ব্রাহ্ম-ঘরের মেয়ে, সেইজন্য আমি ব্রাহ্ম হয়েছি। তবে ঈশ্বরত্বের কল্পনাতে আমি বিশ্বাস করি, সেখানে পৌঁছুতে চেষ্টা করি। জ্ঞানেন্দ্র, সব মানুষ করে, সব মানুষ। ওই ঈশ্বরত্ব। একটি পবিত্র একটি মহিমময় মানুষের মানসিক সত্তায় তার প্রকাশ!
সুমতির ক্ষুদ্রতা, তার ভালবাসার জন্য ধর্মান্তর গ্রহণের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ থেকে মানুষটি কখন চলে আসতেন সর্বজনীন জীবনদর্শনের মহিমময় প্রাঙ্গণে, মুখের সকল বিষণ্ণতা মুছে যেত, এই রক্তসন্ধ্যার আভার মত একটি প্রদীপ্ত প্রসন্ন প্রভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠত মুখখানি। দূর-দিগন্তে দৃষ্টি রেখে মানসলোক থেকে তিনি কথা বলতেন—এখন আমার উপলব্ধি হচ্ছে ঈশ্বরত্বই নিজেকে প্রকাশ করছে মানব-চৈতন্যের মধ্য দিয়ে। God নন, Godliness, yes Godliness, yes; বলতে বলতে মুখখানি স্মিত হাস্যরেখায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠত।
তখন ভারতবর্ষে গান্ধীযুগ আরম্ভ হয়েছে। ১৯৩০ সনের অব্যবহিত পূর্বে। বলেছিলেন গান্ধীর মধ্যে তার আভাস পাচ্ছি। বুদ্ধের মধ্যে তা প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মধ্যে তার ছটা আছে। ওখানে বুদ্ধি দিয়ে পৌঁছুতে পারি; প্রাণ দিয়ে, নিজের শ্রদ্ধা দিয়ে পারি নে। পারি নে। মদ না খেয়ে যে আমি থাকতে পারি নে। আরও অনেক কিছু দুর্বলতা আমার আছে। কিন্তু অন্যের প্রতি অন্যায় আমি করি নে। করব না। ওইটেই প্রথম শিক্ষা। বিচার বিভাগে আমি ওটা প্র্যাকটিসের সৌভাগ্য পেয়েছি। বাঙলায় ওটাকে কী বলব? অনুশীলন? হ্যাঁ তাই। রায় লিখবার সময় আমি সেইরকম রায় লিখতে চেষ্টা করি, লিখি, যাকে বলা যায় ধর্মের বিচার। ডিভাইন জাস্টিস।
ডিভাইন জাস্টিস কথাটা তারই কথা।
–হুজুর!
–চকিত হয়ে জ্ঞানেন্দ্রনাথ ফিরে তাকালেন। বেয়ারা ডাকছে।
–এদিকে কাল রাত্রে একটা সাপ বেরিয়েছে হুজুর। একটু থেমে আবার বললে, তাকে বোধ করি মনে করিয়ে দিলে—অন্ধকার হয়ে গিয়েছে।
মুখ তুলে চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ।
সন্ধে হয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, আবার আকাশে মেঘ দেখা দিয়ে ছ। দূরে দিথলয়ে গ্রামের বনরেখার চিহ্নমাত্র বিলুপ্ত হয়ে গেছে অন্ধকারে, প্রান্তর ব্যাপ্ত করে ক্রমশ গাঢ় হয়ে এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে। বাঙলোর দিকে চাইলেন, আলো জ্বলেছে সেখানে। সুরমাও বাগানে নেই, সে কখন উঠে বাঙলোর ভিতরে চলে গিয়েছে। নিঃশব্দেই চলে গিয়েছে।