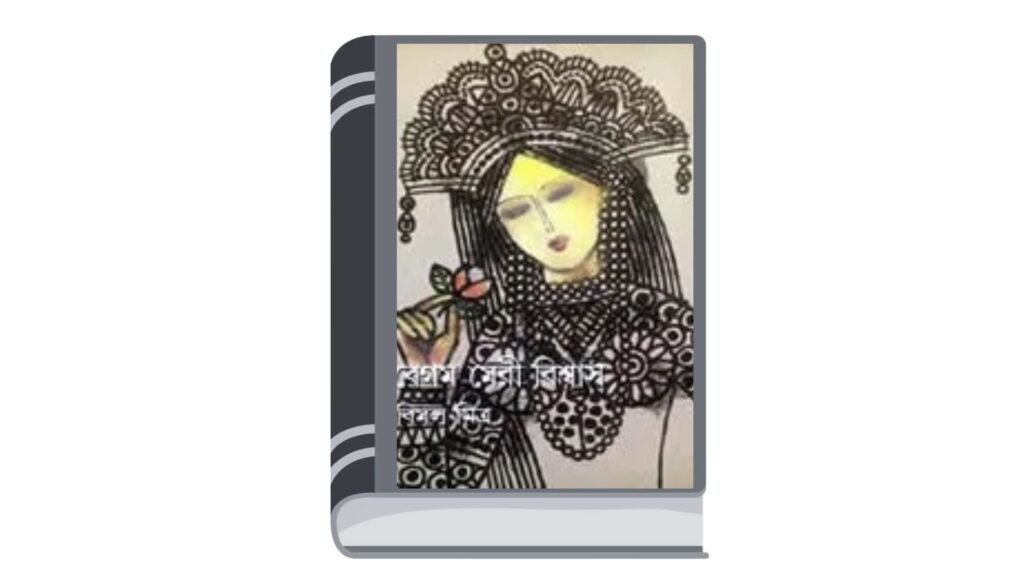১. আদিপর্ব
বেগম মেরী বিশ্বাস – উপন্যাস – বিমল মিত্র
আদিপর্ব
প্রথমে বন্দনা করি দেব গণপতি।
তারপরে বন্দিলাম মাতা বসুমতি ॥
পুবেতে বন্দনা করি পুবের দিবাকর।
পশ্চিমেতে বন্দিলাম পাঁচ পয়গম্বর ॥
উত্তরেতে হিমালয় বন্দনা করিয়া।
দক্ষিণেতে বন্দিলাম সিন্ধুর দরিয়া ॥
সর্বশেষে বন্দিলাম ফিরিঙ্গি কোম্পানি।
কলিযুগে তরাইল পাপী তাপী প্রাণী ॥
দেওয়ান গেল ফৌজদার গেল গেল সুবাদার।
কোম্পানির সাহেব আইল কলির অবতার ॥
ধর্ম কর্ম ইষ্টিমন্ত্র হইল রসাতল।
হরি হরি বল রে ভাই, হরি হরি বল ॥
এখানেই শেষ নয়, আরও আছে। কোন কালে কোন এক নগণ্য গ্রাম্য কবি ছড়া লিখতে গিয়ে সকলকে বন্দনা করে নিজের খ্যাতি অক্ষয় করতে চেয়েছিল। সবটা পাওয়া যায় না। ছেঁড়াখোঁড়া তুলোট কাগজ। গোটা গোটা ভুষোকালিতে লেখা অক্ষর। পড়বার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মনটা একেবারে দু’শো-তিনশো বছর পেছিয়ে চলে যায়। মনে হয়, যেন চোখের সামনে সব দেখছি।
শুধু যুগ নয়, মানুষগুলোও সব আলাদা। সেই খালি গা, মালকোঁচা বাঁধা কাপড়। কারও হাতে লাঠি, কারও গায়ে চাদর। মাথায় কারও আবার টিকি, নইলে ব্রাহ্মণ বলে আপনাকে চিনতে পারব কী করে ঠাকুরমশাই?
আমরা কি আজকের মানুষ নাকি হে? সাতশো বছর আগের আমাদের পরিচয় আমরাই আগে জানতাম না। জানতে পারলাম প্রথম ইবন বতুতার বৃত্তান্ত থেকে। খোরাসানবাসীরা এই বাংলাদেশকে বলত–দুজাখস্ত-পুর-ই-নি-আমত। মানে সুখের নরক। এমন সুখের নরক নাকি সেযুগে আর ভূ-ভারতে কোথাও ছিল না। চূড়ান্ত সস্তাগণ্ডার দেশ। যত ইচ্ছে খাও দাও, ফুর্তি করো। বেশি পয়সা খরচ নেই। বছরে বাড়িভাড়া মাত্র আট দিরাম, মানে বারো আনা। বাজারে চাল-ডাল তেল-নুনের সঙ্গে রূপসি মেয়েও বিক্রি হচ্ছে। বেশি দাম পড়বে না। একটা মোহর দিলেই তোমার কেনা বাদি হয়ে রইল। তোমার বাড়িতে এসে তোমার কাজকর্ম করবে, তোমার গা-মাথা-পা টিপে দেবে। দরকার হলে তোমার বিছানাতেও শোবে। বড় ধর্মভীরু জাত আমরা। আমাদের ওপর দিয়ে তাই কত রকম ঝড়ঝাপটা গেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী।
ইবন্ বতুতা লিখেছেন–have seen no country in the world where provisions are cheaper than this.
মার্কো পোলো, ভাস্কোডাগামা সবাই বাংলাদেশ সম্বন্ধে লিখেছে বটে, কিন্তু সশরীরে আসেনি কেউ এখানে। কিন্তু তাদের লেখা পড়ে এখানে একবার যারা এসেছে তারা আর ফিরে যায়নি। এমন সোনার দেশ কোথায় পাবে শুনি?
এখানকার শুয়োরের মাংস খেয়ে পর্তুগিজরা তো আর নড়তেই চায় না। বলে–ভেরি গুড হ্যাম। এখানকার তাঁতিদের হাতে বোনা কাপড় দেখে বলে–আঃ, ভেরি ফাইন ক্লথ। বাদশা জাহাঙ্গির এই কাপড় পরেছে, বেগম নুরজাহানও এই কাপড় পরেছে। এখান থেকে কাপড় চালান গেছে রোমে, প্যারিসে, বার্লিনে। এবার সোরা। কামান দাগতে গেলে বারুদ লাগে। আর সোরা না হলে আবার বারুদ হয় না। সেই সোরা কিনতে এল ফিরিঙ্গি কোম্পানি। ওলন্দাজ, ফরাসি, পর্তুগিজ আর ইংরেজদের দল।
তারা বললে–আমরা এখানে কারবার করতে এসেছি জাঁহাপনা–আমাদের মেহেরবানি করুন–
বাংলার লাটসাহেব হয়ে এসেছিল বাদশার ছেলে সাহ্ সুজা। সুজার মেয়ের অসুখ। সে আর কিছুতে সারে না। হাকিম হার মেনেছে। কবিরাজও হার মেনেছে। শেষকালে সাহেব ডাক্তারের ডাক পড়ল। ডাক্তার গেব্রিয়াল ব্রাউটনকে ডেকে পাঠানো হল রাজমহলে। বাদশা সাহজাহানের মেয়েকে সারিয়েছে। আর বাদশাজাদার মেয়েকে সারাতে পারবে না! তা কি হয়?
তা সেই যে বাদশার মেয়ের রোগ সারল সেই তখন থেকেই শুরু হল ফিরিঙ্গি পত্তন। বাংলা কি আর ছোটখাটো দেশ গো? না বাঙালিরাই ছোটখাটো জাত। সেই সব অঞ্চলের যত নবাবি আমলা ছিল সকলের কাছে গিয়ে হাজির হল বাদশাহি ফার্মান। ফার্মানে লেখা হল–
জমিদার, চৌধুরী, তালুকদার, মাস্কুদ্দেম, রেকায়া প্রভৃতি
বরাবরেষু–
বাদশার ফার্মান অনুসারে এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, এখন অবধি ইংরাজ কোম্পানি যে-সকল পণ্য জলে ও স্থলে আমদানি ও রপ্তানি করিবে তাহার জন্য কোনও প্রকার শুল্কের দাবি যেন কোনও ইংরাজ কুঠিতে না করা হয়। ইংরেজরা রাজ্যের যে-কোনও স্থানে তাহাদের যে-কোনও পণ্য লইয়া যাইবে বা দেশীয় পণ্য কিনিয়া আনিবে, তাহার শুল্ক কম হইয়াছে বলিয়া যেন তাহা খুলিয়া দেখা বা বলপূর্বক বাজেয়াপ্ত করা না হয়। তাহারা সকল স্থানে বিনা শুল্কে অবাধে বাণিজ্য করিবে। এতদিন তাহাদের নিকট হইতে বন্দরে জাহাজ নোঙর করিয়া থাকার জন্য যেরূপ মাশুল আদায় করা হইত এখন যেন আর তাহাদিগকে সেরূপ না করা হয়। ইত্যাদি ইত্যাদি–
অনেক পুরনো কথা, অনেক পুরনো কাহিনী লেখা রয়েছে তুলোট কাগজের পাতায়। বেশ ভারী পুঁথি। অর্ধেকের ওপর পোকায় খাওয়া, ধুলো জমে জমে ময়লা হয়ে নোনা ধরে গেছে। খেরো খাতায় বাঁধানো ছিল পুঁথিখানা। কার লেখা, পুঁথির নাম কী, তা জানবারও উপায় নেই।
আমি জিজ্ঞেস করলাম–এ পুঁথি আপনি কোথায় পেলেন?
বৃদ্ধ ভদ্রলোক। এককালে অবস্থা ভাল ছিল। বিরাট বাড়ি। সরু-সরু পাতলা-পাতলা নোনা-ধরা ইট। একসঙ্গে পুরো বাড়িটা হয়নি। পুরুষানুক্রমে এক মহলের পর আর এক মহল উঠেছে। একদিকটা নতুন করে মেরামত করা হয়েছে, কিন্তু অন্য দিকের শরিকের হয়তো টাকা নেই তাই সেদিকটা ভেঙে ভেঙে পড়ছে। এক ঘরে রেডিয়ো বাজছে। ইলেকট্রিক লাইটের রোশনাই। আবার ঠিক তার পাশের ঘরটাতেই অন্ধকার ঘুরঘুট্টি। কেরোসিন তেলের হারিকেন জ্বলছে টিমটিম করে। সেই টিমটিমে আলোতেই বাড়ির ছেলেরা মাদুরের ওপর বসে দুলে দুলে নামতা পড়ছে। বাড়ির একতলার ঘরগুলো রাস্তা থেকেও নিচু। যেদিন গঙ্গায় বান ডাকে সেদিন জল ঢুকে পড়ে বাড়ির একতলায় শোবার ঘরে। সেই জলের সঙ্গে কখনও কখনও সাপও ঢোকে। ভাঙা ইটের দেয়াল থেকে কাঁকড়া বিছে বেরিয়ে পড়ে। তখন আর একতলার ঘরে কারও থাকা সম্ভব হয় না। বাক্স-প্যাটরা বিছানা নিয়ে পাশের কোনও শরিকের ঘরে গিয়ে তাদের আশ্রয় নিতে হয়।
কবে এই বংশের কোন আদি পুরুষ এখানে একদিন আস্তানা গেড়েছিলেন। সে হয়তো পলাশীর যুদ্ধের পর কোনও একটা সময়ে। তখন লর্ড ক্লাইভের আমল। লাইব্রেরির পুরনো পুঁথি ঘেঁটে দেখছি, বাদশা দ্বিতীয় আলমগিরের রাজত্বের চতুর্থ বছরে হিজরি ১১৭০ ৫ রবি-উল-শানি, ইংরেজি ১৭৫৭ খ্রি অব্দের ২০ ডিসেম্বর, বাংলা ১১৬৪ সালের পৌষ মাসে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নবাব মিরজাফর খাঁ’র কাছ ণেকে জমিদারস্বরূপ ভেট পান এই ২৪ পরগনা। পরগনা মাগুরা, পরগনা খাসপুর, পরগনা ইক্তিয়ারপুর, পরগনা বারিদহাটি, পরগনা আজিমাবাদ, পরগনা মুড়াগাছা, কিসমত সাহাপুর, পরগনা সাহানগর, কিসমতগড়, পরগনা দক্ষিণ সাগর, আর তারপর পরগনা কলিকাতা। সরকার সাতগাঁ’র অধীনেই কিসমত পরগনা কলকাতা। ইত্যাদি ইত্যাদি—
এই কিসমত পরগনা খুঁজে বার করা মুশকিল। এখনকার ম্যাপে এর নিশানা নেই।
বাদশাহ্ আলমগিরের রাজত্বের চতুর্থ বছরে ১৫ রমজান তারিখে ইংরেজ কোম্পানি আর মিরজাফরের মধ্যে যে সন্ধিপত্র লেখা হল সেখানে অষ্টম আর নবম ধারায় লেখা আছে–
Article VIII–Within the ditch, which surrounds the borders of Calcutta, are tracts of land, beloging to several zemindars; besides this I will grant the English Company six hun dred yards without the ditch.
Article IX–All the land lying to the south of Calcutta, as far as Culpee, shall be under the zemindary of the English Company, and officers of those parts, shall be under their jurisdiction.
The revenue to be paid by them (the Company) in the same manner with other zeminders.
এ হল পরোয়ানা।
এতে খুশি হবার লোক নন ক্লাইভ সাহেব। কোম্পানির সুনাম প্রতিপত্তি হলে তার কী লাভ? ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লাভের সঙ্গে তার তো কোনও সম্পর্ক নেই। কথাটা জাফর আলি খাঁ বুঝলেন। তাই যখন দিল্লির বাদশার সনদ এল তখন দেখা গেল তাতে আর কোম্পানির নাম নেই। তাতে ক্লাইভেরই জয়জয়কার। তখন তাতে আর শুধু শুকনো কর্নেল ক্লাইভ নয়। ক্লাইভের তখন একটা লম্বা-চওড়া পদবি। জবদন্ত-উল-মুলক নাসেরাদ্দৌলা সবত-জঙ্গ বাহাদুর কর্নেল ক্লাইভ। তিনিই তখন দিল্লির বাদশার সনদ পেয়ে ২৪ পরগনার জায়গিরদার জবদস্ত-উল-মুল নাসেরাদ্দৌলা সবত-জঙ্গবাহাদুর কর্নেল ক্লাইভ হয়ে গেছে।
ভদ্রলোক বললেন–ওসব হিস্ট্রির কচকচি আমরা শুনতে চাই না মশাই, আমরা চাল-ডাল-মাছ তরকারির ব্যবস্থা করতে করতেই নাজেহাল, জিনিসপত্তরের যা দাম বাড়ছে তাইতেই আমরা মরে আছি, ওসব পড়বার ভাববার শোনবার সময় কোথায় পাই বলুন?
তারপর বললেন–পুঁথিটার মধ্যে কী পেলেন আপনি?
বললাম–একটা অমূল্য জিনিস পেলাম এর মধ্যে। যা এখন পর্যন্ত কোনও ইতিহাসে পাইনি।
কী রকম?
বললাম পেলাম বেগম মেরী বিশ্বাসের নাম—
তিনি কে?
বললাম–এতদিন এই দুশো বছর ধরে আপনাদের বাড়িতে এ-পুঁথিটা রয়েছে আর একবার এটা পড়েও দেখেননি? দেখলেই জানতে পারতেন বেগম মেরী বিশ্বাস কে?
সত্যিই ভদ্রলোক আসল সংসারী মানুষ। নাম পশুপতি বিশ্বাস। সারাজীবন মামলা করেছেন, অর্থ উপায় করেছেন, যৌবনে ফুর্তি করেছেন, সন্তানের জন্ম দিয়েছেন আর ভাল ভাল খেয়েছেন আর পরেছেন। শরিকদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাবুয়ানি করেছেন। পাড়ার দশজনের মাথার ওপর মাতব্বরি করেছেন। সাধারণত বাংলাদেশের সেকালের আরও নিরানব্বইজন লোক যা করে থাকেন, পশুপতিবাবুও তাই-ই করেছেন। কোথা থেকে এই বাংলাদেশ এল, এ-দেশ আগে কী ছিল, কী করে এই অজ জলাজমি এখনকার বাংলাদেশে পরিণত হল সেসব জানবার আগ্রহ তার কখনও হয়নি। জেনে কোনও লাভ হবে না বলেই আগ্রহ হয়নি। বেশ আছি মশাই, খাচ্ছিদাচ্ছি, বাত-হাঁপানি-ব্লাডপ্রেশার-ডায়াবেটিস নিয়ে অত সব খবর রাখবার সময় কোথায় আমাদের? জানেন, তিন-তিনটে মেয়ের বিয়ে দিয়েছি তিন কুড়িং ষাট হাজার টাকা খরচ করে? ক’জন পারে বলুন আজকালকার বাজারে? প্রথম জামাই মেডিকেল ডাক্তার, সাতশো টাকা মাইনে পায় ডি-ভি-সি’তে, সেকেন্ড জামাই ইঞ্জিনিয়ার….
বাংলাদেশের ইতিহাস জানার চেয়ে নিজের কীর্তিকাহিনী পরকে জানাবার দিকেই পশুপতিবাবুর আগ্রহটা যেন বেশি। সেকালের পুরনো জমিদার বংশ। মাত্র দুশো বছর আগে পর্যন্তই পশুপতিবাবুদের বংশাবলীর কিছু পরিচয় জানা যায়। কোন এক উদ্ধব দাস নাকি এইখানে এই কিসমত পরগনা কলিকাতায় এসে বসবাস শুরু করেন। এখানে এই গঙ্গার ধারে কান্তসাগরে চোদ্দো বিঘে জমির পত্তনি পেয়ে একটা ছোটখাটো বাড়ি করেন। পশুপতিবাবুরা উচ্চরাঢ়ী কায়স্থ। দিল্লির বাদশার কাছ থেকে উদ্ধব দাস ‘খাস বিশ্বাস’ উপাধি পেয়েছিলেন। কিন্তু নিজেদের নামের শেষে শুধু দাস পদবি লেখেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলেই ওই বিশ্বাস পদবিটা চালু হয়ে গেছে। কিন্তু বিয়ে-শ্রাদ্ধ-অন্নপ্রাশনে খাস বিশ্বাস কথাটা এখনও ব্যবহার করতে হয়। ওটা চলে আসছে এবংশে।
ভদ্রলোক তখন অধৈর্য হয়ে উঠেছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন–বেগম মেরী বিশ্বাস আমাদের কেউ হয় নাকি? কী দেখলেন ওতে?
বললাম–সেইটেই তো খুঁজছি–পাতা তো সব নেই, অর্ধেক ছেঁড়া, পোকায় খাওয়া আমার মনে হচ্ছে আপনাদের বাড়িতে যখন এ-পুঁথি পাওয়া গিয়েছে তখন এই পুঁথির লেখকের সঙ্গে আপনাদের নিশ্চয় কিছু যোগাযোগ আছে–
ভদ্রলোক বললেন–সে তো আছেই, কিন্তু বেগম মেরী বিশ্বাসের সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক থাকতে পারে? বেগম তো মশাই মুসলমান–
আমি বললাম–শুধু মুসলমান কেন, মুসলমান তো বটেই, আবার ক্রিশ্চানও বটে, তার ওপর মনে হচ্ছে হিন্দুও–
তারপর বললাম–আমি এক মাসের জন্যে এটা নিয়ে গিয়েছিলাম, তাই ফেরত নিয়ে এলাম, আপনি যদি একটু সময় দেন তো আরও কিছুদিন রেখে পড়ে দেখতে পারি।
ভদ্রলোকের তাতেও আপত্তি দেখলাম না। বলতে গেলে ভদ্রলোকের কাছে এ-পুঁথির কোনওই দাম নেই। পুরনো বাড়ি মেরামত করতে গিয়ে মাটির তলায় আরও অনেক কিছু জঞ্জালের মধ্যে এটা পাওয়া গিয়েছিল। দুশো বছরের পত্তনি এঁদের। তখন এ অঞ্চল জঙ্গলে ভরতি ছিল। চোর-ডাকাতদের ভয়ে তখনকার মানুষ অনেক জিনিসই মাটির তলায় পুঁতে রাখত। খাস বিশ্বাস পদবি যাঁরা পেয়েছিলেন তাঁরা জায়গিরের সঙ্গে কিছু ধনসম্পত্তিও পেয়েছিলেন। সেই ধনসম্পত্তি নিয়েই তারা এসেছিলেন এখানে। ধনসম্পত্তি সে-যুগে লুকিয়ে রাখার জিনিস। কেউ কখনও জানতে পারলে তার আর নিস্তার নেই। উদ্ধব দাস এখানে সেই ধনসম্পত্তি নিয়েই হয়তো একদিন গড়ম্বন্দি তৈরি করলেন। চকমিলানো বাড়ি তৈরি করলেন। ভাবলেন খাস বিশ্বাস বংশ যুগ থেকে যুগান্তর ধরে তার কীর্তিগাথা প্রচার করবে। কিন্তু আস্তে আস্তে বিবাদ শুরু হল শরিকদের মধ্যে, ভাগীরথীর জল শুকিয়ে আসতে লাগল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা দেশের রাজা হয়ে বসল, কুইন ভিক্টোরিয়া থেকে শুরু করে একাদিক্রমে এক-একজন রাজা এসেছে আর খাস বিশ্বাসদের অবস্থা ক্রমান্বয়ে খারাপ থেকে আরও খারাপের দিকে গেছে।
বাড়িতে এসে পুথিখানা পড়তে পড়তে আমার চোখের সামনে থেকে যেন ধীরে ধীরে মহাকালের পরদাগুলো আস্তে আস্তে সরে যেতে লাগল। পয়ার ছন্দে লেখা কাব্য। পয়ারের চৌদ্দটি অক্ষর যেন চৌদ্দ হাজার প্রদীপের আলোর প্রার্য নিয়ে আমার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। এই কলকাতা শহর, এই বিংশ শতাব্দী, এই বাড়ি ঘর রাস্তা, এই সভ্যতা, শিক্ষা, ভণ্ডামি, প্রতিযোগিতা আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জয়ের যুগে আমি সশরীরে যেন আর এক যুগে গিয়ে পৌঁছোলাম। তখন পিচের রাস্তা হয়নি কোথাও। ইলেকট্রিক লাইটও হয়নি। মটর, ট্রেন, প্লেন কিছুই হয়নি। শুধু একটা পালকি চলেছে কালনার মেঠো পথ দিয়ে।
দু’পাশে মাঠ। মধ্যে গোরুর গাড়ি যাবার মতো খানিকটা রাস্তা।
ওপাশ থেকে বুঝি ধুলো উড়িয়ে কারা আসছিল। ঘোড়ার খুরে রাস্তার ধুলো উঠে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। কাছে আসতেই দেখা গেল নবাবের সেপাই তারা। সেপাইরা পালকি থামিয়ে দিলে।
কে? ভেতরে কে আছে?
আজ্ঞে জেনানা!
কাদের জেনানা?
ষণ্ডা-গুন্ডা সেপাই দুটো সোজা কথায় ছাড়বার লোক নয়। মেয়েমানুষের নাম শুনলে জিভ দিয়ে নাল পড়ে ওদের। রোদ টা টা করছে চারদিকে। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাবার জোগাড়। চারজন চারজন আটজন পালকি-বেহারা। পালা করে বয়ে নিয়ে চলেছে। ফেরিঘাটের কাছে একবার একটু জলটল খেয়ে নিয়েছিল বেহারারা। ফেরিঘাটের নৌকোর মাঝিও একবার কান্তকে একা পেয়ে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করেছিল–পালকিতে ইনি কে কত্তা?
এমনিতে সন্দেহ হবারই কথা। অন্তত একটু কৌতূহল। মানে সঙ্গে তো আর কোনও স্ত্রীলোক নেই। একলা-একলা এই পথেঘাটে এমন রূপসি মেয়েমানুষ দেখলে মানুষের জানতে ইচ্ছে হয় বই কী! দিনমানই হোক আর রাতবিরেতই হোক, মেয়েমানুষ যায় নাকি এমন করে!
কান্ত জবাব দিয়েছিল–আমাদের হাতিয়াগড়ের রানিবিবি!
কথাটা শুনে বুড়ো মাঝির কোথায় কৌতূহল নিবৃত্তি হবে, তা নয়; চোখ দুটো যেন আরও বড় বড় হয়ে গেল। হাতিয়াগড়ের জমিদারগিন্নির তো পালকিতে যাবার কথা নয়। গেলে নৌকোতে যাবেন। জমিদারের নিজেরই তো বজরানৌকো আছে। এই ফেরিঘাটেই কতবার বাবুর বজরা বাঁধা হয়েছে।
আপনারা?
কান্ত বললে–আমরা নবাব সরকারের লোক—
কথাটা শুনেই বুড়ো মাঝি গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। লম্বা একটা সেলাম করেছিল সসম্ভ্রমে। সম্ভ্রমে বটে ভয়েও বটে। মুর্শিদাবাদের নিজামত নবাব সরকারের কথা শুনলে কার না ভয় হয়। ভয়েই বোধহয় আর কোনও কথা বলেনি বুড়ো মাঝিটা। ঘন ঘন সেলাম করেছিল। দুটো সেপাই সঙ্গে ছিল। আর ছিল আটজন পালকি-বেহারা। আর কান্ত নিজে। এইসব এত লোকের বহর দেখেই মাঝিটার সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু কথাটা শোনবার পর আর বাক্যব্যয় করেনি। পালকিসুদ্ধ নদীপার করে দিয়ে আর একটা লম্বা সেলাম করেছিল কান্তকে।
তারপর আর কিছু ঘটেনি। এতদূর আসার পর আবার সেই সেপাই।
কাদের জেনানা?
পালকির ভেতরে যে গুটিসুটি মেরে চুপ করে বসে ছিল, কথাটা বুঝি তার কানেও গেল। মাথার ঘোমটাটা সে একটু নামিয়ে দিলে। একলা-একলা চুপ করে বসে থাকতে পা ব্যথা হয়ে গিয়েছিল। এতক্ষণ বাইরে থেকে কেবল পালকি-বেহারাদের হুস-হাস শব্দ ছাড়া আর কিছু ছিল না।
শোনা গেল সঙ্গের লোকটা বলছে–আমাদের হাতিয়াগড়ের রানিবিবি।
কোথায় যাবে?
মুর্শিদাবাদ, চেহেল্-সুতুন।
পাঞ্জা?
বাইরের আর কোনও কথা শোনা গেল না ভেতর থেকে।
হাতিয়াগড়ের জমিদারগিন্নি উদগ্রীব হয়ে কান পেতে রইল। কেউ আর কিছু বললে–না। সেপাই দুটো বোধহয় পাঞ্জা দেখে খুশি। কেউ আর পালকির দরজা খুলে পরীক্ষা করতেও চাইলে না। তারপর কেবল বেহারাদের হুস-হাস শব্দ। সারা শরীরটা দুলছে সেই সকাল থেকে। নদীতে যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ বেশি কষ্ট হয়নি। নৌকোর ঘরের মধ্যে একা-একা কেটেছে। ওরা বাইরেই ছিল। বাইরেই ওরা খেয়েছে, বাইরেই ঘুমিয়েছে। আর সেপাই দুটো পাহারা দিয়েছে কেবল বসে বসে।
হঠাৎ দরজাটা ফাঁক হয়ে গেল।
সেই লোকটা সসম্ভ্রমে মুখ বাড়িয়ে বললে–এখানে আপনাকে নামতে হবে রানিবিবি, আমরা কাটোয়ায় পৌঁছে গেছি—
*
সেকালের কাটোয়া কেমন জায়গা, পুঁথির মধ্যে তার বেশ বর্ণনা আছে। চারিদিকে মাঠ। মাঠের মধ্যে একটা জায়গায় এসে কয়েকটা বটগাছ চারিদিকটা বেশ ছায়াচ্ছন্ন করে রেখেছে। দু-একটা আটচালা। একটা শিবমন্দিরও ছিল। ভাঙাচোরা অবস্থা তার। ঠিক তার পাশেই একটা বাড়ি। পোড়া ইটের পাকা বাড়ি। আর পাশেই গঙ্গা।
এককালে এখানে বর্গিরা এসে হাঙ্গামা বাধিয়েছিল! লুঠপাট করে সব শ্মশান করে দিয়ে গিয়েছিল। সে কয়েক বছর আগেকার কথা। এখন কাছাকাছি গ্রামের চিহ্ন নেই। গ্রামের লোক সেই সময়ে এ-গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল আর আসেনি। কয়েকটা বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল বর্গিরা। খেতের ফসল কেটে নিয়ে গিয়েছিল। গোরুছাগল কিছু নিতে বাকি রাখেনি। সেসব এক দিন গিয়েছে। কান্তর মনে আছে সে-সব দিনের কথা।
সে ছিল বড়চাতরা।
খুব ছোট তখন সে। ভাল করে মনে পড়ে না সব কথা। এক-একদিন রাত্রে হইহই করে গা-ময় চিৎকার উঠত। বর্গি এল’ বর্গি এল’ বলে রব উঠত। দিদিমা ঘুম ভাঙিয়ে দিত। বলত–কান্ত ওঠ–
বর্ষার রাত। নাজিরদের ডোবাটার পাশ থেকে ঝিঁঝি পোকার ডাক আসছে অনবরত। গোলপাতার চালের বাতায় দিদিমা বড় বড় কাঁঠাল ঝুলিয়ে রাখত। যে কাঁঠাল পাকেনি, সেই কাঁঠাল বাতি হলেই গোপালকে দিয়ে দিদিমা গাছ থেকে পাড়িয়ে রাখত। তারপর চালের বাতায় দড়ির শিকেয় ঝুলিয়ে রাখত। সেই কাঁঠাল থেকে দু-তিন দিন বাদেই গন্ধ বেরোত। পেকে ভুরভুর করত গন্ধ। গন্ধ পেয়ে হলদে হলদে বোলতা এসে জুটত কোত্থেকে।
তখন কান্ত ছোট। অতদূরে হাত পৌঁছুত না। একটা কচার লাঠি দিয়ে কাঁঠালটার গায়ে লাগাতেই তার মধ্যে লাঠিটা ঢুকে যেত, তখন কাঁঠালটা পেকে একেবারে ভুসভুসে হয়ে গেছে।
দিদিমা দেখতে পেয়ে বলত–কে রে? কাঁঠালটা কে খোঁচালে রে? তুই বুঝি?
শুধু কি কাঁঠাল? আমগাছও ছিল কান্তদের। অত আম কে খাবে তখন! খাবার মধ্যে তো কেবল দিদিমা আর সে! তক্তপোশের তলায় পাকা আমগুলো আমপাতার ওপর সাজিয়ে সাজিয়ে রাখত দিদিমা। রোজ রোজ বেছে বেছে পাকা আমগুলো দিয়ে জলখাবার হত নাতির। সেই পেট-ভরা আম খেয়ে দোয়াত কালিকলম তালপাতা নিয়ে পাঠশালায় যেত কান্ত। স্বরে অ আর স্বরে আ দিয়ে বাংলা হাতের লেখা মকশো করতে হত। কাঁধে আঁকড়ি ক, মুখে বাড়ি খ,…
কিন্তু সেবার সত্যি সত্যিই রাতদুপুরে বর্গিরা এল। নাজিরদের বাড়ির দিকে সকলে দৌড়োচ্ছিল। দিদিমা বুড়ো মানুষ, বেশি জোরে হাঁটতে পারে না। চৌধুরীবাবুদের বুড়ো কর্তা বাতের ব্যথায় পঙ্গু হয়ে পড়েছিলেন বিছানায়। তিনি আর দৌড়োত পারলেন না, ধপাস করে মাটিতে পড়ে মরে গেলেন। চৌধুরীবাড়ির নবউ পেছনে ছিল, শ্বশুরকে পড়ে যেতে দেখে ন’বউ থেমে গেল। শাশুড়ি তখন এক নাতির হাত ধরে আর এক নাতিকে কোলে নিয়ে দৌড়াচ্ছে।
কর্তাকে পড়ে যেতে দেখে শাশুড়ি গিন্নি বললে–উনি থাকুন নবউমা, তুমি চলো, পোয়াতি মানুষ তুমি, তুমি আগে নিজের পেরান সামলাও—
বুড়োকর্তা সেখানেই পড়ে রইলেন। চৌধুরীবাড়ির বড়কর্তা, মেজকা, সেজকর্তা, নকর্তা তখন বাড়ির বড় বড় লোহার সিন্দুকগুলো ধরে ধরে সেই ডোবা পুকুরের মধ্যে ডুবোচ্ছে। চৌধুরীবাবুদের অবস্থা ভাল। রুপোর থালাবাসন ছিল, সোনার বাট ছিল, সমস্ত সেই রাত্তিরে পুকুরের পাকের মধ্যে পুঁতে ফেললে। তারপর লাঠি-সড়কি নিয়ে মাথার ওপর ঘোরাতে ঘোরাতে চার ভাই বেরিয়ে পড়ল।
আর শুধু কি চৌধুরীরা?
বড়চাতরার যত লোক ছিল সব পালিয়ে বাঁচত বাড়িঘর ছেড়ে। চাল-ডাল-নুন তেল ফেলে রেখে শুধু প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে গ্রাম-কে-গ্রাম উজাড় হয়ে যেত! কোথায় যেত তার ঠিক নেই। নাজিরদের বাড়িটায় একতলায় মাটির নীচেও ঘর ছিল। নাজিররা সেখানেই লুকিয়ে থাকত।
দিদিমা বলত–তুই যেবার হলি সেবারও বর্গি এইছিল, তোকে কোলে নিয়ে তোর মা আর আমি নাজিরদের বাড়ির তলায় গিয়ে লুকোলুম–
খুব ছোটবেলায় দিদিমার কাছে এইসব গল্প শুনত। শুধু দিদিমা কেন, সে-গল্প বড় চাতরার সবাই জানত। ওই পাঠশালার পশ্চিম দিকের কালাচাঁদের মঠ পেরিয়ে যেখানে বিরাট একটা ঝাকড়া-মাথা বটগাছ হা হা করে আকাশের দিকে হাত তুলে বোশেখ-জষ্ঠি মাসের বিকেলবেলার দিকে তুমুল কাণ্ড করে বসে, তারও ওপাশে রাজবিবির মসজিদ, সেই রাজবিবির মসজিদ ছাড়ালেই সরকারি সড়ক। সেই সড়ক দিয়ে সোজা হেঁটে গেলেই তিন দিনের মধ্যে রাজমহল পৌঁছিয়ে যাবে। নাজিরবাবুদের সর্দার পাইক দফাদার ওই সরকারি সড়ক দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে আসত। চৌধুরীবাবুরা যখন একবার কাশীধামে গিয়েছিল, তখন ওই পথ ধরেই গিয়েছিল। গিয়ে পাটনার গঙ্গা থেকে নৌকো নিয়েছিল। আর ঠিক ওই রাস্তা বরাবরই বর্গিরা আসত। একেবারে পঙ্গপালের মতো হুড়মুড় করে এসে ঢুকে পড়ত বড়চাতরায়। ঠিক যখন খেতের ধান কাটবার সময় হত, সেই সময়ে কোত্থেকে এসে হাজির হত আর তারা চলে যাবার পর খাঁ খাঁ করত সমস্ত বড়চাতরা।
বড়চাতরার লোকে কান্নাকাটি করত গা দেখে। কতবার ঘর-বাড়ি-গোলা মরাই-খেত-খামার সমস্ত জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়ে গেছে বর্গিরা।
দিদিমাও কাঁদত। বলত–ওই হারামজাদারা তোর বাবাকেও খুন করে ফেলেছিল রে।
ওই সময়েই কী একটা হাঙ্গামায় মা গেল। রইল শুধু দিদিমা আর সে। দিদিমা বুড়ি মানুষ। কতদিন আর বাঁচবে! তবু যেক’দিন বেঁচে ছিল, ততদিন নাতির জন্যে অনেক করে গেছে। নাজিরদের চণ্ডীমণ্ডপে বরদা পণ্ডিতের পাঠশালা ছিল একদিকে, আর একদিকে ছিল সারদা পণ্ডিতের মক্তব। সারদা পণ্ডিত নিজে পড়াতেন না ছাত্রদের, মৌলবি রেখেছিলেন। মৌলবি ফারসি পড়াত পড়ুয়াদের।
নাজিরবাবু বলেছিলেন–কনেবউ, তুমি আবার নাতিকে ফারসি পড়াতে গেলে কেন বলল তো? সংস্কৃত পড়লে কি বিদ্যে হয় না?
দিদিমা বলেছিল–না কর্তাবাবু, তা নয়, নাতি চিরকাল চাষাভুষো হয়ে থাকবে, তা কি ভাল?
তা ফারসি শিখে তোমার নাতি নবাব সরকারে নায়েব-নাজিম হবে নাকি?
দিদিমা বলেছিল–নায়েব-নাজিম না হোক, নায়েব-নাজিমের খেদমদগার তো হতে পারবে? ফারসিটা শিখলে তবু সরকারি চাকরি অন্তত একটা তো পাবে।
তা নবাব-সরকারের চাকরিতে আর সে-গুড় ছিল না তখন। নবাব আলিবর্দি খাঁ নিজেই নবাব-সরকারের চাকরিতে ঢুকেছিল বলে নবাব হতে পেরেছিল মুর্শিদাবাদের। ওই মহারাজ রাজবল্লভ, পেশকার হয়ে ঢুকে মহারাজ। ওই রামনারায়ণ, জানকীরামের কাছে সরকারি চাকরি করেছিল বলেই পাটনার দেওয়ানি পেয়ে গিয়েছিল।
দিদিমার আশা ছিল অনেক। আশা ছিল নিজের জামাই তার যে-আশা মেটাতে পারেনি, বাপ-মা মরা নাতি তাই পারবে। কিন্তু দিদিমা যদি জানত যে শেষকালে তারই নাতি কিনা চাকরি নেবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দপ্তরে!
কিন্তু সে-কথা এখন থাক!
কাটোয়ার কাছে আসতেই পালকি-বেহারারা থেমে গেছে। সেই সক্কালবেলা খেয়া পার হয়ে বেহারারা ছুটতে শুরু করেছে দুটো চিড়ে-মুড়কি মুখে দিয়ে। তারপর আর বিরাম নেই।
নিজামত-সরকারের তলব পেয়ে কাটোয়ার কোতোয়াল সব ব্যবস্থাই করে রেখেছিল। পালকিটা পোঁছোতেই ফৌজি সেপাই দুটো সামনে এসে খাড়া হল।
কান্তও তৈরি ছিল। পাশেই পাকাবাড়িটা। কোতোয়ালের লোক সামনেই হাজির ছিল। কান্ত এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে ঘর সাফ হয়েছে?
কোতোয়ালের লোক কান্তকে সেলাম করে বললে–হ্যাঁ হুজুর—
রান্নাবান্নার কী ব্যবস্থা?
সব তৈরি হচ্ছে হুজুর। বারোজনের রান্নার হুকুম দিয়েছেন কোতোয়াল।
রান্না করছে কারা? হিন্দু না মুসলমান?
হুজুর, মুসলমান!
কান্ত একটু অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে–কেন? মুসলমান কেন? হাতিয়াগড়ের রানি তো হিন্দু বিবি, মুসলমানের হাতের রান্না খাবেন কেন? হিন্দু রসুইয়ের বন্দোবস্ত হয়নি?
তা জানিনে হুজুর।
কান্ত বললে–ঠিক আছে, বিকে ডেকে দাও, রানিবিবিকে নিয়ে ভেতরে যাক, তারপরে আমি কোতোয়াল সাহেবের সঙ্গে কথা বলছি–
ঝি নয়, বোরখা পরা বাঁদি বেরিয়ে এল রানিবিবিকে নামিয়ে নিয়ে যেতে। পালকির দরজা ফাঁক হতেই কান্ত দেখলে সলমাচুমকির ওড়না দিয়ে রানিবিবি মাথায় একটা ঘোমটা দিয়েছিল। পালকি থেকে মাথা নিচু করে বেরোতে গিয়েই ঘোমটাটা খসে গেল মুখ থেকে। আর কান্ত এক পলকে দেখে ফেললে রানিবিবির মুখখানা। দুপুরের রোদে মুখখানা লাল হয়ে গেছে। ফরসা রঙের ওপর লালচে আভা বেরোচ্ছে সারা মুখখানাতে। আর কপালের ঠিক মধ্যিখানে সিঁথির ওপর জ্বলজ্বল করছে মেটে সিঁদুর।
ফৌজি সেপাই দুটো সেইদিকে চেয়ে দেখছিল। পালকি-বেহারারাও দেখছিল। সেই তাদের দিকে নজর পড়তেই কান্ত নিজেই যেন কেমন অপরাধী মনে করলে নিজেকে। তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে মুখখানা খানিকক্ষণের জন্যে অন্তত ভোলবার চেষ্টা করলে।
*
সারা পুঁথিখানায় এমনি সব বর্ণনা। ধুলো আর নোনা হাওয়া আর পোকার হাত থেকে পুঁথিখানাকে রক্ষে করা যায়নি। বাংলাদেশের জল-হাওয়াতে মানুষই বলে তাড়াতাড়ি মরে যায়, তায় আবার তুলোট কাগজ।
তুমি আমি এবং আর পাঁচজন যখন দু’শো বছর ধরে ইংরেজ রাজত্বে বাস করে সেকালের সব ইতিহাস ভুলে বসে আছি, তখন এমন একখানা পুঁথি কোথায় মাটির তলায় আমাদের চোখের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে ছিল তার হিসেব রাখবার প্রয়োজন বোধ করিনি! একদিন মুর্শিদাবাদ থেকে রাজধানী কলকাতায় চলে এসেছিল, তারপর কলকাতা থেকে দিল্লি। এই দু’শো বছরে শুধু যে যুগই বদলেছে তাই নয়, মানুষ বদলেছে, মানুষের মতিগতিও বদলেছে। আর মানুষই বা কেন, ভূগোলও বদলে গেছে। এখন যে-গঙ্গা হিমালয় থেকে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত এসে এখানে পদ্মা নাম নিয়েছে, আসলে তা পদ্মাই নয়। আসলে তা ছিল সমুদ্র। সমুদ্র থেকে একদিন দ্বীপ জেগে উঠেছে, নতুন জনপদ যেমন সৃষ্টি করেছে, নতুন নদীও তাতে সৃষ্টি হয়েছে। রামায়ণের যে-গঙ্গা সাতটা ধারায় বয়ে গিয়েছিল, তার তিনটে স্রোত পুব দিকে গিয়ে নাম নিয়েছিল হ্লাদিনী, পাবনী আর নলিনী। আর পশ্চিম দিকে যে-তিনটে ধারা বয়ে গিয়েছিল, তার নাম সুচক্ষু, সীতা আর সিন্ধু। বাকি স্রোতটা মাঝখান দিয়ে ভগীরথের পেছন-পেছন সমুদ্রে গিয়ে পড়েছিল। এই স্রোতটার নামই গঙ্গা। ইংরেজরা যখন এল তখন গঙ্গার নাম বদলে তার নাম রাখলে কাশিমবাজার নদী। কাশিমবাজার পর্যন্ত কাশিমবাজার নদী, যেখানে ভাগীরথী জলাঙ্গীর সঙ্গে এসে মিশেছে। বাকিটা হল হুগলি নদী। আর এখন তো সবটাই হুগলি নদী।
এই হুগলি নদীরই কি কম নাম-ডাক! এই নদীটা দিয়েই একদিন নবাবের সেপাইয়া বর্গিদের সঙ্গে লড়াই করতে গেছে। এই নদীটা দিয়েই একদিন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সোরার নৌকো জাহাজ বোঝাই করে বিলেতে মাল পাঠিয়ে দিয়েছে। এই নদীটা দিয়েই একদিন হাতিয়াগড়ের জমিদার মুর্শিদাবাদের সরকারে খাজনা জমা দিতে এসেছে। এই গঙ্গার পাড়ের ওপরেই কিরীটেশ্বরীর মন্দির। মুর্শিদকুলি খাঁ’র কানুনগো দর্পনারায়ণ এই কিরীটেশ্বরীর মন্দির নতুন করে গড়ে দিয়ে নিজের দেবভক্তি প্রচার করেছিলেন। ঢাকা থেকে ফিরে যতদিন ডাহাপাড়ায় বাস করেছিলেন ততদিন এই মন্দিরের তত্ত্বাবধানের দিকে লক্ষ রেখেছিলেন। এইখানেই আছে রাঙামাটি। এখানকার মাটি লাল। হিউ-এন-সাং তার ভ্রমণবৃত্তান্তে যাকে বলেছেন কর্ণসুবর্ণ, এই রাঙামাটিই সেই কর্ণসুবর্ণ। মহারাজ দাতাকর্ণের অন্নপ্রাশনের সময় বিভীষণ এখানে স্বর্ণবৃষ্টি করেছিলেন, তাই নাকি এর নাম হয়েছিল কর্ণসুবর্ণ। কে জানে! কত রকম গল্প জড়িয়ে আছে এই দেশকে ঘিরে, সব লিখতে গেলে এ-বইও মোটা হয়ে যাবে, তখন আপনারাও বিরক্ত হয়ে যাবেন, আমারও স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাবে রাত জেগে লিখে লিখে।
এই যে নলহাটি আজিমগঞ্জ লাইনে সাগরদিঘি নামে একটা ইস্টিশন, ওর পেছনেও একটা গল্প আছে। কিন্তু সে-গল্প থাক। এবার অন্য একটা গল্প বলি। সাগরদিঘি থেকে চার ক্রোশ উত্তর-পুবে একটা গাঁ আছে, তার নাম এক-আনি চাঁদপাড়া। গৌড়ের সিংহাসনে একদিন হোসেন সাহ্ জবরদস্ত নবাব বলে বিখ্যাত হয়েছিলেন। সেই হোসেন সাহেবের বাবা এই চাঁদপুরে এসে উঠেছিলেন। কিন্তু অবস্থা বৈগুণ্যে চাকরি নেন এক ব্রাহ্মণের কাছে। চৈতন্যচরিতামৃতে ওই ব্রাহ্মণের নাম সুবুদ্ধি রায় বলে লেখা আছে। লোকে সুবুদ্ধি রায়কে চাঁদ রায় বলে ডাকত। চাঁদপাড়ার কাজি হোসেন সাহের গুণের পরিচয় পেয়ে নিজের মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিলেন। একদিন যে ছিল সুবুদ্ধি রায়ের আশ্রিত, সে-ই আবার একদিন গৌড়ের রাজ-সিংহাসন আলো করে বসল। কিন্তু সুবুদ্ধি রায়ের কথা হোসেন সাহ ভোলেননি। নবাব হয়েই চাঁদপাড়া গ্রামটার স্বত্ব সুবুদ্ধি রায়কে এক আনা খাজনায় দিয়ে দিলেন। তখন থেকেই সেই গ্রামের নাম হয়ে গেল এক আনি চাঁদপাড়া।
কিন্তু আজ যে রাজা আবার কালই হয়তো সে ফকির হয়ে যাবে। একদিন সুবুদ্ধি রায়ের ক্ষমতা এমনই বেড়ে উঠল যে, তখন হোসেন সাহই বা কে জগদীশ্বরই বা কে! সেই সুবুদ্ধি রায়ই একদিন চাবুক মেরে হোসেন সাহের গায়ে দাগ বসিয়ে দিলেন। আর যায় কোথায়! হোসেন সাহ কিছু বললেন না, কিন্তু তার বেগম বড় চটে গেলেন।
স্বামীকে বললেন–এত বেয়াদপি কাফেরের?
হোসেন সাহ বললেন–তা হোক, একদিন তো রায়মশাইয়ের খেয়ে-পরেই মানুষ হয়েছি–
ওসব যুক্তিতে ভুললেন না বেগম সাহেবা। তিনি বললেন–সুবুদ্ধি রায় যা-ই হোক, ও হল কাফের, কাফেরকে খুন করলে কোনও গুণাহ হয় না–
শেষে বেগমের কথাও রইল, সুবুদ্ধি রায়ের সম্মানও রইল। হোসেন সাহ একদিন আচমন করতে করতে সুবুদ্ধি রায়ের গায়ে জল ছিটিয়ে দিলেন। সেই জল তার মুখে গিয়ে লাগল। এরপর সুবুদ্ধি রায় আর সংসারে থাকেননি। সংসার ত্যাগ করে মহাপ্রভুর নামে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।
এ তো গেল পাঠান আমলের কথা। সেই হোসেন সাহই বা কোথায় তলিয়ে গেল। তার জায়গায় শেষ নবাব এল দায়ূদ খাঁ। পাঠান আমলের ইতি হল এই দায়ূদ খাঁর আমলেই। মানসিংহ এসে হাজির বাংলার সুবেদার হয়ে। মোগল-পাঠানে লড়াই হল এই গঙ্গার ধারেই সেরপুর আতাই-এ! এই সেরপুর আতাইতেই পাঠানদের হাতির দল পালিয়ে বাঁচল। সেই মানসিংহের সঙ্গেই একজন ব্রাহ্মণ বাংলাদেশে এসেছিলেন। তিনি কান্যকুজের লোক, জিঝোতিয়া বংশের ব্রাহ্মণ। মানসিংহের সৈন্য তিনিই পরিচালনা করতেন। তাঁর নাম সবিতা রায়। এই সবিতা রায়ই বর্তমান জেমো রাজবংশের আদিপুরুষ। এই বংশের জয়রাম রায় কপিলেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সে-মন্দিরও এই গঙ্গার গর্ভেই চলে গেছে।
এ-গঙ্গা নিয়েছেও যেমন অনেক আবার দিয়েছেও অনেক। এই গঙ্গাই ঘসেটি বেগমকে নিয়েছে, আমিনা বেগমকে নিয়েছে। নানিবেগম, ময়মানা বেগমকে নিয়েছে। লুৎফুন্নিসা বেগমকেও নিয়েছে। আর দিয়েছে এই মরালীকে। এই মরিয়ম বেগমকে। এই বেগম মেরী বিশ্বাসকে। এই যে-বেগম মেরী বিশ্বাসের গল্প এখানে আপনাদের বলতে বসেছি।
তা এই গঙ্গার পাড় ধরেই হাতিয়াগড়ের রানিবিবির পালকিটা এসে থামল কাটোয়ার সরাইখানার সামনে। কোতোয়ালের হেফাজতে ছিল এ-বাড়িটা। নবাব আলিবর্দি খাঁ একবার বর্গিদের তাড়িয়ে দিয়ে এসে নানিবেগমকে নিয়ে এক রাত্রের জন্যে এখানে উঠেছিলেন। সবরকম বন্দোবস্তই আছে এখানে। দরকার হলে এখানকার খিদমদগার গরম জলের ব্যবস্থা করতে পারে স্নানের জন্যে। খাবার বলল খাবার, বিছানা বলো বিছানা, এমনকী তেমন দরকার হলে মদের ব্যবস্থাও করতে পারে।
কান্তর ঘাড় থেকে যেন বোঝাটা নামল।
সেপাই দুজনও ঘাড়ের বন্দুক নামিয়ে গায়ের মুখের ঘাম মুছে নিলে। অনেক দূর পথ হেঁটে এসেছে। তাদের খিদে পাবার কথা। গাছতলাটায় বসল গিয়ে দু’জন।
ও কান্তবাবু! কান্তবাবু—
কান্ত কোতোয়ালের সঙ্গে দেখা করে খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্তের কথা বলতে যাচ্ছিল। হাতিয়াগড়ের রানি হিন্দুবিবি, মুসলমানের হাতের রান্না কেমন করে খাবে! তা ছাড়া, এখানে কতদিন থাকতে হবে, এখান থেকে মুর্শিদাবাদ যাবার আবার কী বন্দোবস্ত করা হয়েছে, তাও জানা দরকার। নবাব সরকারের চাকরির অনেক ল্যাটা। কোথাও কেউ মুখ খুলে কথা বলবে না। সবাই যেন সবাইকে সন্দেহ করে। অথচ যখন ফিরিঙ্গি কোম্পানিতে চাকরি করত তখন এসব ছিল না। বেভারিজ সাহেব তোক ভাল। কান্তকে বাবু বলে ডাকত। তিন টাকা করে মাইনে দিত সাহেব, কিন্তু মাইনেটা কম হলে কী হবে, সাহেব সেটা পুষিয়ে দিত নানাভাবে। সোরা বেচে বেশি লাভ হলে সেবার বকশিশ দিত। তা বকশিশ না দিলেও চাকরি না করে উপায় ছিল না কান্তর। বেভারিজ সাহেব চাকরি না দিলে কোথায় থাকত সে? বাঁচত কী করে? খেত কী? বড়চাতরা থেকে সেই যে সেবার প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছিল, তারপরে কি আর সেখানে গিয়ে ওঠা যেত। গাঁ-কে-গাঁ যেন আগুন জ্বেলে পুড়িয়ে দিয়েছিল তারা।
সে এক ভয়ংকর কাণ্ড!
সেইবারই বেশি করে কাণ্ডটা হল।
ওই রাতদুপুরে আবার একদিন হইহই রইরই চিৎকার উঠল। বড়চাতরার তাবৎ লোক ঘুম ভেঙে যে-যেদিকে পারল ছুটল। কিন্তু সেবার বোধহয় একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। নাজিরদের বাড়িটার ওপর তখন ঝাঁপিয়ে পড়েছে বর্গিরা। নাজিররাই বড়চাতরার বর্ধিষ্ণু লোক। বাড়িতে চিরকাল ধান, চাল, গুড়, নুন মজুত করা থাকে। তা সবাইকার জানা। তাই সেবার আর নাজিররা রেহাই পেতো না। দু-একটা গাদা বন্দুক বোধহয় ছুঁড়েছিল নাজিরবাবুর দিশি সেপাই। কিন্তু সে আর কতটুকু। কান্তরা যখন ঘুম ভেঙে উঠেছে তখন নাজিরদের বাড়িটা দাউদাউ করে জ্বলছে।
সুতরাং পুব দিকে দৌড়োও। পালাও পালাও।
যার যেদিকে চোখ গেছে সেই দিকেই পালিয়েছে। শেষকালে সেই ঘুরঘুটি অন্ধকারে দৌড়োতে দৌড়োতে একেবারে সোজা গঙ্গা। গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কাটতে কাটতে একেবারে কলকাতায়। কলকাতায় বেভারিজ সাহেবের সোরার গদিবাড়ি গঙ্গার ঘাটের ওপর। সকালবেলা সেখানে গিয়েই দাঁড়িয়েছিল কান্ত। আর তো কেউ নেই তখন তার। আর কলকাতাতে কে থাকবে কার, গোটাকয়েক চালাঘর, কয়েকটা পাকা বাড়ি ফিরিঙ্গিদের কোম্পানি তখন সেই জলাজঙ্গলেই বেশ কায়েম হয়ে উঠেছে।
বেভারিজ সাহেব তখন পালকিতে চড়ে গদিবাড়ি দেখতে এসেছে।
জিজ্ঞেস করলে–হু আর ইউ? টুমি কে?
তখন কান্ত ইংরেজি বুলি জানত না। কিছু ফারসি পড়েছে সারদা পণ্ডিতের মক্তবে, আর কিছু বাংলা বরদা পণ্ডিতের পাঠশালায়। অথচ আশ্চর্য, শেষকালে সেই কান্তই বেশ গড়গড় করে সাহেবদের সঙ্গে ইংরেজি বুলি আউড়ে যেত। চাকরিতে টিকে থাকলে কান্তর আরও উন্নতি হত হয়তো। বেভারিজ সাহেবের নেকনজরে পড়ে অনেক কিছু করে নিয়েছে। কিন্তু কাল হল বশির।
বশির মিঞা একদিন জিজ্ঞেস করেছিল–কত তলব পাস তুই এখেনে?
তিন টাকা।
বশির মিঞা নবাব-সরকারের লোক। নিজামতের পেয়ারের নোকর। চুড়িদার পায়জামার ওপর চুনোট করা মলমলের পিরান পরে। কাঁধে আবার কলকার কাজ। বাহারে টেড়ি, পান-জর্দা কিমাম খেয়ে মুখ লাল করা থাকে সবসময়। তলবের অঙ্ক শুনে হো হো করে হেসে উঠল। বললে–দুর। নবাব-নিজামতের খেদমতগার পর্যন্ত রোজ তিন টাকা আয় করে।
কীসে আয় করে?
রিশশোয়াত! ঘুষ! তোর নোকরিতে ঘুষ আছে?
কান্ত বললে–না, শুধু বকশিশ দেয় সাহেব–
তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে উঠল বশির, ঘুষ না হলে নোকরি করে ফয়দা কী? আমি তো তিনটে বিবি রেখেছি ওই ঘুষের জোরে। তলব তো পাই দশ টাকা। দশ টাকায় তিনটে বিবি পোষা চলে? তুই-ই বল না? তিন বিবির নোকর-নোকরানি আছে, বিবিদের বায়নাক্কা কি কম নাকি? সরাবের একটা মোটা খরচা আছে, পান-তামাকু কোনটা নেই? দশ টাকায় চলে কী করে?
কান্তও বশিরের বড়লোকিপনার বহর শুনে হতবাক।
জিজ্ঞেস করলে–তুই দশ টাকায় চালাস কী করে?
বশির মিঞা বললে–ঘুষ নিয়ে–
তোকে ঘুষ দেয় কেন লোকে?
ঘুষ না দিলে নবাব কাছারিতে কারও কাজ হোক দিকিনি দেখি!
তুই কি কাছারিতে কাজ করিস?
আরে না, নিজামতের খাস মোহরার আমার ফুপা। আমার ফুপাকে বলে দিলে তোরও নোকরি হয়ে যাবে নিজামতে–! তুই নোকরি নিবি?
কিন্তু বেভারিজ সাহেব যে আমাকে খুব ভালবাসে। গদিবাড়ির চাবি যে আমার হাতে থাকে।
বশির মিঞা কান্তর বোকামি দেখে হাসবে কি কাদবে বুঝে উঠতে পারলে না।
আরে নিজামতের নোকরির কাছে ফিরিঙ্গি সাহেবের নোকরি? ওরা তো বিলাইত থেকে কারবার করতে এসেছে। সোরা কিনবে সুতো কিনবে আর দরিয়ার ওপারে চালান দেবে। ওদের কোম্পানি যখন উঠে যাবে তখন কী করবি? তখন বেভারিজ সায়েব তোকে খিলাবে? তখন তো ফ্যা ফ্যা করে নোকরির চেষ্টায় ঘুরে বেড়াবি মুর্শিদাবাদের দফতরে–ওরা তো আর হিন্দুস্তানে মৌরসিপাট্টা নিয়ে জমিনদারি করতে আসেনি–
কান্ত খবরটা শুনে সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ফিরিঙ্গি কোম্পানি কারবার গুটিয়ে কালাপানি পাড়ি দিয়ে চলে যাবে?
তা যাবে না? ওরা তো পয়সা লুঠতে এসেছে, পয়সা না পেলেই চলে যাবে। পয়সা না পেলে কেউ ঝুটমুট পড়ে থাকে? আবার যেখানে পয়সা কামাবে সেখানে চলে যাবে। ওদের কী? ওরা বেনের জাত, পয়সা কামিয়ে পাততাড়ি গুটিয়ে একদিন চলে যাবে। তখন ভো-ভ-মাঝখান থেকে তোর নোকরিটা খতম হয়ে যাবে
সেই বশির মিঞার কথাতেই বলতে গেলে কান্ত বেভারিজ সাহেবের চাকরি ছেড়ে দিয়ে এই নিজামত সরকারের চাকরিতে ঢুকেছে।
বশির মিঞা বলেছিল–মন দিয়ে টিকে থাক তুই, এখন নতুন নবাব হয়েছে, আমার ফুপার বড় ইয়ার মনসুর-উল-মুলক সিরাজ-উ-দ্দৌলা শা কুলি খান বাহাদুর হেবাত জঙ আলমগির–
তা সেই চাকরিতে ঢুকতে-না-ঢুকতে প্রথম হুকুম হয়েছে হাতিয়াগড় থেকে সেখানকার রানিবিবিকে মুর্শিদাবাদের হারেমে নিয়ে আসতে হবে। এনে কী হবে, কিছুই বলে দেয়নি বশির মিঞা। নিজামতের হুকুম হচ্ছে হুকুম। দুটো সেপাই দিয়েছে কোতোয়ালি থেকে তার সঙ্গে, পালকি দিয়েছে, পালকি-বেহারা দিয়েছে, নিজামতি পাঞ্জা দিয়েছে।
ও কান্তবাবু!
সেপাই দুটো গাছতলা থেকে ডাকছিল কান্তকে। কিন্তু তার আগেই সরাইখানার ভেতর থেকে মিহি গলায় আর একটা ডাক এল।
বাবুজি!
সেই বাঁদিটা। বোরখার মুখের ঢাকনাটা ঈষৎ খুলে তাকে ডাকছে।
কান্ত কাছে গেল। আমাকে ডাকছ নাকি?
বিবিজি গোসলখানায় গিয়েছিল, খানার কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম, বলছেন, বাবুজিকে ডেকে আন!
আমাকে? কেন?
তা জানি না হুজুর।
মুসলমানি খানা খাবেন না বুঝি? তা আমি তো সেই জন্যেই কোতোয়ালিতে যাচ্ছি হিঁদু খানার বন্দোবস্ত করতে–
বাঁদি বললে–না, তা নয় হুজুর, বিবিজি মুসলমানি খানা খাবেন আমাকে বলেছেন।
মুসলমানি খানা খাবে? হাতিয়াগড়ের রানিবিবি হিন্দুর মেয়ে হয়ে মুসলমানের ছোঁয়া খাবে? তুমি ঠিক বলছ?
জি হাঁ–আপনি ভেতরে আসুন, বিবিজি আপনার সঙ্গে একবার মোলাকাত করবেন আপনি আসুন
কান্ত একটু আড়ষ্ট হয়ে উঠল। তারপর সামলে নিয়ে বলল–আচ্ছা। চলো–
*
ঠিক এই পর্যন্ত এসেই পাতাটা শেষ। এর পর আর নেই। অনেক খুঁজে খুঁজেও আর পাওয়া গেল না। পুরনো পুঁথি পড়ার এই একটা অসুবিধে। যেখানে ঠিক কৌতূহলটা ঘন হয়ে আসছে সেই জায়গাটাই বেছে বেছে পোকায় কাটে, সেই জায়গাটাই বেছে বেছে হারিয়ে যায়।
হঠাৎ পশুপতিবাবুর একটা চিঠি পেলাম।
তিনি লিখেছেন–বাড়ি মেরামত করতে গিয়ে পুঁথির আরও অনেকগুলো পাতা পাওয়া গিয়েছে, আপনি একবার এসে দেখে যাবেন—
পুরনো পুঁথি নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন তারা জানেন, এর মধ্যে অনেক রকম ভেজাল থাকে। একজন চণ্ডীদাস শেষকালে দশজন চণ্ডীদাসে পরিণত হতে পারে। তখনকার দিনে ছাপাখানা ছিল না। একহাজার পাতার একখানা পুঁথি একজন নকলনবিশকে পাঁচটা টাকা আর একখানা বাঁধিপোতা গামছা দিলেই নকল করে দিত। তারপর তার মধ্যে নিজের বিদ্যে বুদ্ধি শিক্ষা অশিক্ষা ঢুকিয়ে দিলে কারও
আর কিছু ধরার উপায় থাকত না।
কিন্তু এ-পুঁথি অন্যরকম। এ কবি নিজের হাতেই লিখেছেন বলে মনে হল। এমন কিছু বিখ্যাত কবিও নন। নকলনবিশের হাতের ছোঁয়াচ কোথাও পাওয়া গেল না। আর পশুপতিবাবু নিজেই বলছেন তাদের পূর্বপুরুষ উদ্ধব দাস। খাস বিশ্বাস হলেও দাসই বটে। কিন্তু কবি বিনয়ী। বৈষ্ণব পদকর্তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে উদ্ধব দাসও নিজেকে ভক্ত হরিদাস বলে ঘোষণা করেছেন। দাসানুদাস। তিনি নিজে কিছুই নয়। নিজের জন্যে তিনি কিছুই করেননি। এই জমি, এই সম্পত্তি, এই ভোগ-ঐশ্বর্যবিলাস তার কিছুই তার প্রাপ্য নয়। তিনি এই সংসারে ঈশ্বরের কৃপায় এসেছিলেন আবার একদিন ঈশ্বরের কৃপাতেই বিদায় নেবেন। এ-সংসারে কে কার? এ-সংসারই তো তার লীলাভূমি গো।
আমার খুব আগ্রহ ছিল এই বেগম মেরী বিশ্বাস সম্বন্ধে কিছু জানতে। কে এই মেরী বিশ্বাস। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসে লর্ড ক্লাইভের সঙ্গে এই বেগমের কীসের সম্পর্ক। এই হাতিয়াগড়ের রানিবিবিই বা কে? যে কান্ত ছেলেটি নিজামত নবাব-সরকারের হুকুম পেয়ে কোনও হিন্দু রানিবিবিকে নিয়ে কাটোয়ার সরাইখানাতে উঠল, ও-ই বা কে? উদ্ধব দাসই বা এদের কথা জানল কী করে? সে এত বড় মহাকাব্য লিখতে গেল কেন? যে-ইতিহাস ছোটবেলা থেকে পাঠ্যপুস্তকে পড়ে এসেছি এর সঙ্গে তো তা মিলছে না। উদ্ধব দাস এ ইতিহাস কোথায় পেলে?
পড়তে পড়তে অনেক রাত হয়ে এল। তারপর কলকাতার অন্ধকার ঘরের মধ্যে একে একে পৃথিবীর সমস্ত লোক ঘুমিয়ে পড়ল। শুধু আমি একলা জেগে রইলাম, আর জেগে রইল ইন্ডিয়ার অষ্টাদশ শতাব্দী। অষ্টাদশ শতাব্দীর সেই পৃথিবী থেকে আর্তকণ্ঠের এক করুণ চিৎকার ভেসে উঠল। সে কান্না সেদিন কেউ শুনতে পায়নি। আলিবর্দির হারেমের মধ্যে সেই একক-কান্না এত বছর পরে আবার যেন পুঁথির পাতা বেয়ে আমার কানে এসে পৌঁছোল। কে কাঁদছে? আজকে চারিদিকে যখন সবাই হাসছে, তখন কাঁদছে কে?
কোথাও তো কেউ জেগে নেই। অষ্টাদশ শতাব্দী, উনবিংশ শতাব্দী, বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পেরিয়ে এসেও আমরা তো সবাই ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। যারা পাহারা দেবার ছিলেন তারা সবাই তো বিদায় নিয়েছেন। রামমোহন বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথ, কেউ নেই পাহারা দেবার। মাঝখানে দু’দুটো বড় যুদ্ধ আমরা পার হয়েছি। দু’শো বছর ব্রিটিশের তবে কাটিয়ে আমাদের মেরুদণ্ড বেঁকে গিয়েছে। আমরা নির্বিঘ্নে অনাচার করছি, অত্যাচার করছি, চুরি করছি, ব্ল্যাকমার্কেট করছি, লোক-ঠকানোর কারবারে আমরা বেশ রীতিমতো পাকা হয়ে উঠেছি। ঘটনাচক্রে আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে বটে, কিন্তু আমরা তো স্বাধীন হইনি। দারিদ্র্য আর অভাব আর অনাচার থেকে তো মুক্তি পাইনি। কিন্তু তবু তো আমরা কেউ-ই কঁদিনি। তবে এমন করে আজ কাঁদছে কে?
অথচ আমরাই এতদিন খদ্দর পরেছি, চরকা কেটেছি, লবণ সত্যাগ্রহ করেছি। এতদিন মেদিনীপুরে একটার-পর-একটা বিলিতি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবদের গুলি করে মেরেছি। রাইটার্স বিল্ডিংয়ে ঢুকে সাহেবদের খুন করে কঁসি গিয়েছি। পাড়ায় পাড়ায় লাঠিখেলা কুস্তি করার আখড়া বানিয়েছি। বন্দে মাতরম’ শুনলে আমাদের রক্ত নেচে উঠেছে। সেসব কথা তো স্বাধীন হবার পর আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম। ১৯৪৭ সালের পর থেকে আমি আর পশুপতিবাবুরা তো খদ্দর পরা ছেড়েই দিয়েছি। লুকিয়ে লুকিয়ে বিলিতি জিনিস কিনতে পেলে বর্তে গিয়েছি। লাঠিখেলা আর কুস্তির আখড়া তুলে দিয়ে সেখানে আমরা সরস্বতীপুজো করি। পুজোর ঠাকুরের সামনে আমরা লাউডস্পিকার লাগিয়ে সিনেমার সস্তা গান মাইক্রোফোনে বাজাই। আমরা ধুতি ছেড়ে দিয়ে সরু-পা-ওয়ালা প্যান্ট পরি। ট্র্যানজিস্টার-সেট কাঁধে ঝুলিয়ে মডার্ন হয়ে ঘুরে বেড়াই। কাঁদবার তো আমাদের সময় নেই! তবে এমন করে আজ কাঁদছে কে?
হঠাৎ নজরে পড়ল বিরাট দমদম হাউসের এককোণে বেগম মেরী বিশ্বাস একা জেগে জেগে কাঁদছে।
উদ্ধব দাস তাঁর কাব্যের শেষ সর্গে শান্তিপর্বের ভেতর বেগম মেরী বিশ্বাসের যে-চিত্র এঁকেছেন তা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। অষ্টাদশ শতাব্দীর মানুষ আজ এই বিংশশতাব্দীর মানুষের মতোই সেদিন নিজেদের বুঝতে পারেনি। একদিন হাতিয়াগড়ের রানিবিবিকে পরোয়ানা পাঠিয়ে নবাবের হারেমের মধ্যে এনে পুরেছে। সে ছিল লালসা আর রূপের আকর্ষণ। মেয়েমানুষের দেহ আর অর্থ উপার্জনের কলাকৌশল আয়ত্ত করাকেই সেদিন চরম মোক্ষ বলে জ্ঞান করেছে সবাই। টাকা চাই। যেমন করে হোক টাকা চাই-ই। জীবন অনিত্য। এই জীবদ্দশাতেই আমার ভোগের চরম পরিতৃপ্তি চাই। বাদশার কাছ থেকে পাওয়া খেতাব চাই। নবাবের পেয়ারের পাত্র হওয়া চাই। তা হলেই বুঝলাম আমার সব চাওয়া-পাওয়া মিটল। তা হলেই বুঝলাম আমার মোক্ষ লাভ হল।
ঠিক এই অবস্থায় বেগম মেরী বিশ্বাস কাঁদছে কেন?
মানুষ যা চায় সব তো পেয়েছিল মরিয়ম বেগমসাহেবা। গ্রামের অখ্যাত এক নফরের মেয়ে হয়ে জন্মে একদিন চেহেল-সুতুনের বেগমসাহেবা হয়েছিল। তারপরে হল কর্নেল ক্লাইভের প্রিয়পাত্রী। তখন কর্নেল ক্লাইভ মানেই বাংলা মুলুকের নবাব। তবু কেন সে কাঁদে?
মরিয়ম বেগমসাহেবারা যে কেন কাঁদে তা জানতে হলে উদ্ধব দাসের কাব্যের আরও অনেক পাতা, ওলটাতে হবে।
যে-কান্ত একদিন নিজামতের হুকুমত পেয়ে হাতিয়াগড়ের হিন্দু রানিবিবিকে এই চেহেল্-সুতুনে নিয়ে এসেছিল তাকে আর তখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বশির মিঞা ছুটোছুটি করছে চারদিকে। সেই কাফের কান্তটা কোথায় গেল?
ওদিকে চারদিকে কড়া পাহারা বসেছে। চেহেল সুতুনের ভেতর থেকে কোনও জিনিস না বাইরে বেরিয়ে যায়। মিরজাফর আলি সাহেব কড়া হুকুম দিয়ে দিয়েছে কোতোয়ালিতে। হারেমের ভেতরে খোঁজা-সর্দার পিরালি খাঁ তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে বেগমসাহেবাদের ওপর। বাইরে থেকে জাল পাঞ্জা নিয়ে কেউ যেন না ভেতরে ঢুকতে পারে। যদি কেউ ঢুকে পড়ে তো তাকে সোজাসুজি মিরজাফর আলি সাহেবের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। ফিরিঙ্গি কোম্পানির কাছ থেকে হুকমত এসেছে যতক্ষণ না কর্নেল ক্লাইভ সাহেব নিজে এসে তদন্ত করেন ততক্ষণ একটি জিনিসও কারও সরাবার এক্তিয়ার নেই। এ হুকুমতের নকল বাইরেও পাঠানো হয়েছে। মুৎসুদ্দিয়ান, কানুনগোয়ান, চৌধুরীয়ান, করোরিয়ান, জমিদারান পংনসরৎসাহী ওরফে হাতিয়াগড় সরকার ও পং হোসেন প্রতাপ সরকার সিলেট জায়গির নবাব সমসদ্দৌলা সুবে বাংলা। তোমরা সকলে অবগত হও যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্নেল ক্লাইভ মুর্শিদাবাদে আগত হইতেছেন। উক্ত দিবসে উক্ত মুৎসুদ্দিয়ান, কানুনগোয়ান, চৌধুরীয়ান, করোরিয়ান, জমিদারান, প্রভৃতি সকলে তাহার নিকট হাজিরা দিয়া সরকারি হুকুমতের মর্যাদা নির্বাহ করিবা।
মোতালেক মুসুবাদ কাজির দেউড়ি,
–জনাব মনসুর আলি মেহের মোহরার ॥
এই পরোয়ানা বেরোবার পর থেকেই সবাই উদগ্রীব হয়ে বসে আছে। এবার কী হবে! এবার কে নবাব হবে! যে নবাবকে খুন করেছে তার কী হবে! কিন্তু কারও মুখে কোনও কথা নেই। সবাই ভয়ে। ভয়ে মুখ বন্ধ করে ঘরের ভেতরে দরজায় হুড়কো এঁটে বসে আছে।
তবু রাস্তাতেও ভিড়ের কমতি নেই। মনসুরগঞ্জ-হাবেলিতে এসে উঠেছে মিরজাফর আলি খাঁ। উঠেছে তার ছেলে মিরন আলি খাঁ। ফটকের সামনে কড়া পাহারা বসে গেছে। বন্দুক কাঁধে নিয়ে তারা দিন রাত পাহারা দেয়। জগৎশেঠজি আসে, হাতিয়াগড়ের ছোটমশাই আসে, ডিহিদার রেজা আলি আসে, মেহেদি নেসার আসে। পরামর্শ আর ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হয়। কে নবাব হবে, ক্লাইভ সাবে কাকে নবাব করবে! লোকের কৌতূহলের শেষ নেই!
বহুদিন আগে একদিন একটা পালকি এসে থেমেছিল চেহেল্-সুতুনের ফটকে। নিজামতের চর কান্ত সরকার সেদিন পালকিটাকে চেহেল সুতুনের ফটক পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে নিজের আস্তানায় চলে গিয়েছিল। আর কেউ জানত না সে-ঘটনাটার কথা। বড় গোপনে সে ব্যাপারটা সমাধা হয়েছিল বশির মিঞার সঙ্গে। কিন্তু যারা জানত না তারা একটু কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল। নবাবি হারেম। সে বড় তাজ্জব জায়গা। আগে কান্ত সরকারের এ-সম্বন্ধে কোনও ধারণা ছিল না। এত তার অলিগলি, এত তার কানুন-কিসমত। দুনিয়ার সমস্ত আইন-কানুনের বাইরে যেন চেহেল্-সুতুন। সেখানে খুন হয়ে গেলেও নবাবের খেদমতে তার কোনও আর্জি নেই। অন্ধকারে সেখানে তোমাকে গলা টিপে খুন করে মেরে ফেললেও কেউ প্রতিকার করবার নেই। সেখানে তুমি যদি একবার যাও তা হলে আর কখনও বাইরে আসবার কথা মুখে আনতে পারবে না। ইন্তেকাল পর্যন্ত তুমি সেখানে বন্দি হয়ে রইলে।
পালকিটা গিয়ে চবুতরার সেই কোণের দিকে দাঁড়াল।
কান্ত সেই দিকেই সেদিন হাঁ করে তাকিয়ে ছিল। বশির মিঞার কথাতে যেন তার ঘুম ভাঙল।
বশির মিঞা বললে–লে চল, ওদিকে আর দেখিসনে, নবাবের মালের দিকে নজর দিতে নেই, কেউ জানতে পারলে তোর গর্দান যাবে!
কথাটা কানে গিয়ে বিধেছিল খট করে।
কী বললি তুই?
বশির হেসে উঠল খিলখিল করে। চোখ মটকে বললে, নবাবের মাল—
তার মানে?
কান্তর আপাদমস্তক রিরি করে উঠল।
কী বলছিস তুই? ও তো হাতিয়াগড়ের রানিবিবি! ও তো হিন্দু বিবি রে—
বশির মজা পেয়ে গেল। বললে–হিন্দুদের বিবিরাই তো মজাদার মাল রে—
কান্তর মনে হল এক চড়ে বশির মিঞার মুখখানা ঘুরিয়ে দেয়। এমন জানলে কি আর সে রানিবিবিকে এমনভাবে এত দূর রাস্তা সঙ্গে করে পাহারা দিয়ে আনত। বশির মিঞা হয়তো রসিকতার চোটে ভুলেই গিয়েছিল যে কান্ত হিন্দু। কান্তর দিদিমা মুসলমানদের ছুঁয়ে ফেললে গঙ্গায় স্নান করে ফেলত। বড়চাতরার জমিদারবাবুরা ফৌজদারের কাছারিতে নাজিরের চাকরি করত বটে, কিন্তু সেরেস্তার কাজ সেরে বাড়িতে এসে কাপড়-পিরেন সব ছেড়ে ফেলত। তারপর স্নান করে শুদ্ধ হত। আর কান্ত আজ নিজামতে চাকরি করতে এসেছে বলে একথাও মুখ বুজে সহ্য করতে হল।
কিন্তু নবাবের কি মেয়েমানুষের অভাব যে হাতিয়াগড়ের রানিবিবিকে খুঁজে এনে এখানে চেহেল্-সুতুনে পুরতে হবে?
অভাব হবে কেন? তুই বড় বেকুবের মতো কথা বলিস! একটা মেয়েমানুষে কি কারও চলে? এই দ্যাখ না, আমার তো তিন-তিনটে আওরাত। একটু একঘেয়ে লাগলেই মুখ বদলে নিই। দুনিয়ায় মেয়েমানুষের পয়দা হয়েছে কেন বল তো?
তার মানে?
এরকম অদ্ভুত প্রশ্ন কান্তর মাথায় কখনও আসেনি। এ নিয়ে আলোচনা করতেও তার যেন একটু লজ্জা হল।
বশির মিঞা বললে–না, তোর জানা দরকার, নবাবদের এত বেগম থাকে কেন! খোদাতালার বেহেস্তে যেমন হুরি-পরি থাকে নবাবদের হারেমেও তেমনি বেগম বাদি থাকে। কেউ আসে খোরাসান থেকে, কেউ কান্দাহার থেকে, কেউ চাটগাঁ থেকে, কেউ কালাপানির ওপার থেকে।আমার তলব বাড়লে। আমি তো ইয়ার ঠিক করেছি একটা ইহুদি আওরাত রাখব। ইহুদি আওরাত দেখেছিস?
কান্তর বিরক্তি লাগছিল। বললে–ওসব কথা থাক এখন–
সেদিন ওই পর্যন্ত কথা হয়েছিল বশির মিঞার সঙ্গে। হাতিয়াগড়ের রানিবিবিকে চেহেল সুতুনের ভেতরে পাঠিয়ে দিয়ে সেদিনকার মতো কান্তর ছুটি হয়ে গিয়েছিল। আবার কোনও নতুন হুকুম হলেই বশির মিঞা তাকে জানাবে বলেছিল। কিন্তু তারপর হুড়মুড় করে সব কী যেন ঘটে গেল। তখন যা কিছু ঘটেছে সব তার চোখের আড়ালে। তখন সে বেগম সেজে বোরখা পরে চেহেল সুতুনের ভেতরে লুকিয়ে আছে মরিয়ম বেগম সেজে।
তখন সবাই জানে কান্তই মরিয়ম বেগম। বোরখা পরার পর কেউ আর তাকে চিনতে পারেনি।
মরিয়ম বেগমকে ধরবার জন্যে তখন সমস্ত মুর্শিদাবাদে তোলপাড় পড়ে গেছে। কোথায় মরিয়ম বেগমসাহেবা? মরিয়ম বেগমসাহেবা কোথায়?
মুর্শিদাবাদে এসে পৌঁছেছে কর্নেল ক্লাইভ। জোর হুকুম দিয়েছে? মরিয়ম বেগমসাহেবাকে চাই।
অথচ চেহেল্-সুতুনের ভেতরে অন্য সব বেগমসাহেবারা তখন সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে সুরমা দিয়েছে। বুকে কাঁচুলি পরেছে। পায়ে পাঁয়জোড়। সবাই সার বেঁধে অপেক্ষা করছে কখন কার ডাক পড়বে আম-দরবার থেকে।
কিন্তু তখনও কাঁদছে কে?
মনে আছে একদিন আবার কান্ত গিয়ে হাজির হয়েছিল বশির মিঞার কাছে।
বশির মিঞা বলেছিল–আবার তোর কীসের দরকার?
কান্ত বলেছিল–একটা কথা ছিল তোর সঙ্গে। একটু আড়ালে আসবি, চুপি চুপি বলব—
বশীরের যেন এসব কথা শোনবার সময়ও ছিল না। আগ্রহও ছিল না। তার তখন অনেক কাজ। তাড়াতাড়ি বললে–তোর নোকরির কথা আমি কিছু বলতে পারব না।
আমি চাকরির কথা বলছি না–
নোকরির কথা বলছিস না তো কী কথা বলছিস?
চাকরির কথা কান্তর কিছু বলবার ছিলও না। বড়চাতরা থেকে একদিন যখন চলে এসেছে তখন তার কাছে ফিরিঙ্গি কোম্পানি যা, নবাব-নাজিমও তাই। চাকরিই হয়তো তার কপালে নেই। যেমন অনেক জিনিসই তার কপালে নেই। এখন মুর্শিদাবাদের মসনদে কেউ বসুক আর না বসুক, তাতে কিছুই আসে যায় না তার।
কী বলবি জলদি বল!
সেই হাতিয়াগড়ের রানিবিবিকে সেদিন নিয়ে এসেছিলাম, তার কথা বলছি—
সে তো হারেমে আছে। তার সঙ্গে তোর কীসের দরকার ইয়ার?
তার সঙ্গে একটু দেখা করতে পারলে ভাল হত—
তোর কি মাথা খারাপ! তুই হারেমের মধ্যে যাবি? খোঁজা-সর্দার তোর গর্দান রাখবে?
কান্তর মুখখানা আরও করুণ হয়ে উঠল। বললে–তুই চেষ্টা করলে পারিস, তোর ফুপা মনসুর আলি সাহেব থাকতে কেউ তোকে কিছু বলবে না–তোর হাত দুটো ধরে বলছি ভাই, একটু দয়া কর তুই–
হঠাৎ বশির মিঞার কেমন সন্দেহ হল।
কেন বল তো? তোর এত টান কেন? তুই কি রানিবিবিকে দেখেছিস নাকি?
হ্যাঁ
কী করে দেখলি? সেপাই দিয়ে বোরখা পরিয়ে আনবার কথা ছিল, দেখলি কী করে? মুখ দেখেছিস?
হ্যাঁ!
বশির মিঞা যেন খেপে লাল হয়ে উঠল। এই জন্যেই তো কাফেরদের দিয়ে এইসব কাজ করাতে চায়নি মনসুর আলি সাহেব। নেহাত পীড়াপীড়ি করলে বশিরটা, তাই এই কাজের ভার দেওয়া। কোথা থেকে কোন হিন্দুর বাচ্চাকে ধরে এনে কিনা বললে–একে নোকরি দাও–!
বশির মিঞার তখন সত্যিই অনেক কাজ। মাথা ঘুরে যাবার মতো অবস্থা। নবাব মারা যাবার পর থেকে চারদিক থেকে শকুনেরা এসে ওত পেতে বসে আছে লুঠের মালে ভাগ বসাবে বলে। মহম্মদি বেগ নিজে মাল সাবাড় করেছে, সুতরাং তারই যেন পাওনাটা বেশি! ওটা কে না করতে পারত? নবাবকে ধরে দুটো হাত দড়ি দিয়ে বেঁধে একটা চাকু বুকের ওপর চালিয়ে দিয়েছে। একবার দু’বার তিনবার। একবারেই মামলা ফতে হয়ে গিয়েছিল। তবু সাবধানের মার নেই। হাত দুটো খুনে লাল। ভেবেছিল, মিরনের যখন দোস্ত সে, তখন দোস্তালির হকদার হতে পারবে সে। কিন্তু সে গুড়ে বালি। হকদার এই কদিনেই অনেক পয়দা হয়েছে। সবাই মিরজাফর আলি খাঁ’র দিকে হা করে চেয়ে আছে। সে-ই যেন বেহেস্তের আফতাব পাইয়ে দেবে!
কান্ত বললে–একটিবার শুধু দেখা করিয়ে দে ভাই বশির আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল রানিবিবি
তোর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল? বলছিস কী তুই? তুই রানিবিবির সঙ্গে কথাও বলেছিস নাকি–?
হ্যাঁ!
যেন অমার্জনীয় অপরাধ করে ফেলেছে কান্ত, এমনি করে তার দিকে চাইলে বশির।
তুই যে কথা বলেছিস এটা কেউ জানে? কেউ দেখেছে?
কান্ত বললে—না—
কেউ দেখেনি তো?
না, আমি লুকিয়ে দেখা করেছি—
কিন্তু তুই তো জানিস নবাবের হারেমের বিবিদের সঙ্গে কারও মোলাকাত করার এক্তিয়ার নেই, দেখা করা গুনাহ–
কান্ত বললে–কিন্তু আমাকে যে রানিবিবি ডেকে পাঠিয়েছিল ভাই–আমার কী দোষ।
তোকে ডেকে পাঠিয়েছিল? কোথায়? কী জন্যে?
কান্ত বললে–কাটোয়াতে!
কী কথা বললে রানিবিবি?
এবার যেন বশির মিঞাও কান্তকে হিংসে করতে লাগল। এমন জানলে বশির মিঞা নিজেই তো হিন্দু কাফের সেজে রানিবিবিকে নিয়ে আসত। কিন্তু ওদিক থেকে হুকুম ছিল, রানিবিবিকে আনতে পাঠাবার জন্যে যেন নবাব-নিজামত সরকারের হিন্দু আমলা পাঠানো হয়। নইলে এসব কাজের জন্যে কখনও লোকের অভাব হয় নাকি।
বলব তোকে সব, আল্লার-কিরে বলছি সব বলব, কিন্তু তার আগে আমাকে একবার দেখা করিয়ে দে রানিবিবির সঙ্গে। হারেমের ভেতরে গিয়ে একবার শুধু বাইরে থেকে একটা কথা বলে আসব–
কী কথা?
কান্ত বললে–কাটোয়ার সরাইখানার সামনে একটা পাগলা নোক এসে সেদিন খুব গান গেয়েছিল, সবাই খুব খুশি তার গান শুনে, রানিবিবি তার নামটা জানতে চেয়েছিল আমার কাছে। আমি নামটা জেনে এসে আর বলতে পারিনি তাকে। বলবার সুযোগ হয়নি–
কে সে লোকটা?
সে একটা পাগলা কছমের লোক। কিন্তু খুব মজাদার গান গাইতে পারে ভাই। আমাকে তার নামটা জেনে আসতে বলেছিল রানিবিবি। নামটা জেনেও এসেছিলাম, কিন্তু রানিবিবিকে তা বলা হয়নি সেইটে একবার হারেমের ভেতরে গিয়ে বলে আসব–একবার শুধু যাব ভেতরে, আর নামটা রানিবিবিকে বলেই চলে আসব–মাইরি বলছি, ভেতরে আমি থাকব না বেশিক্ষণ–
বশির মিঞা চুপ করে কী যেন ভাবতে লাগল।
এই তোর পায়ে পড়ছি ইয়ার, আজকে একবার দেখা না করতে পারলে হয়তো জীবনে আর দেখা করা হবে না। অথচ কথা দিয়ে কথা রাখতে পারলুম না বলে মনটায় বড় আফশোস হচ্ছে ভাই, এ আফশোস আমার মরণেও যাবে না–
কিন্তু লোকটা কে? কার নাম জানবার জন্যে রানিবিবির এত নাফড়া?
কান্ত বললে–বলছি তো একটা পাগলা-ছাগলা লোক—
জাসুস নয়তো?
জাসুস? তার মানে?
ফিরিঙ্গিদের গোয়েন্দা ফোয়েন্দা নয়তো? ওরা তো চর লাগিয়েছে তামাম মুর্শিদাবাদে–
আরে না, জাসুস হতে যাবে কেন? চরই বা হবে কেন?
তা নাম কী তার?
উদ্ধব দাস!
নামটা শুনে কিছুই বোঝা গেল না। মনসুর আলি মেহের সাহেবের মোহরার দফতরে ওনামের কোনও চর তো নেই। সকলের নামই মুখস্থ করে রেখেছে বশির মিঞা। উদ্ধব দাস তা হলে হয়তো কোনও বাউল-ফকির হবে। বাউল-ফকিরদের মুলুক এই বাংলা মুলুক। সব বাঙালির বাচ্চাই বাউল-ফকির ভেতরে ভেতরে। ওরা রাজ্য চায় না, মসনদ চায় না, আওরাত চায় না, দৌলত চায় না, শুধু চায় আল্লাতালার দোয়া। তাজ্জব জাত এই বাঙালির বাচ্চারা। আল্লাতালার নাম করতে করতে বাদশাহি পর্যন্ত চলে গেলেও এদের খেয়াল থাকে না।
বশির মিঞা বললে–আচ্ছা চল, খোঁজা-সর্দারকে বলে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছি তোকে, কিন্তু হুঁশিয়ার, বেশিক্ষণ থাকবি না
কান্ত বললে–না ভাই বশির, কথা দিচ্ছি বেশিক্ষণ থাকব না—
তারপর কোণের ফটকটার কাছে গিয়ে বললে—আয়–
ফটকের সামনে পাহারা দিচ্ছিল কে একজন। বশির মিঞা তাকে পাঞ্জা দেখাতেই ভেতরে যেতে দিলে। লম্বা সুড়ঙ্গ মতন রাস্তা। মাথার ওপরে পাতলা ইটের ছাদ। সেটা পেরিয়ে আর একটা ফটকের কাছে আসতেই আর একজন মুখোমুখি দাঁড়াল। বশির মিঞা বুক ফুলিয়ে এগিয়ে গেল। ভয়ডর কিছু নেই। এই পথ দিয়েই হারেমে যাবার রাস্তা। দু’পাশে ঘুলঘুলির মতন গর্ত। ঘুলঘুলির মধ্যে পায়রা বাসা বেঁধেছে। সামনে দিয়ে কারা আসছে। তারা বাইরে যাবে।
বশির মিঞা পাহারাদারকে জিজ্ঞেস করলে–পিরালি কোথায় রে?
লোকটা কী যেন বললে। বশির মিঞা তাকে একপাশে ডেকে কানে কানে কী বলতে লাগল। হাত-মুখ নেড়ে দু’জনের কী সব কথাও হল। দূর থেকে কান্ত কিছুই শুনতে পেলে না। বশিরের ইঙ্গিতে কাছে যেতেই বশির বললে–দেখিস হুঁশিয়ার, ঝটপট চলে আসবি, আর তোর কাছে টাকা আছে?
কান্ত বললে–টাকা? কীসের টাকা?
টাকা লাগবে না? তোকে ঢুকতে দিচ্ছে যে, পিরালিকে ঘুষ না দিলে যে চেয়েই দেখবে না তোর দিকে–
টাকা তো সঙ্গে নেই, তলব পেয়ে পরে দিতে পারি।
বশির মিঞা বললে–দুর, নগদ ছাড়া ঘুষ হয় কখনও! ঘুষের কারবার কখনও বাকিতে চলে?
বলে নিজের পিরানের জেব থেকে টাকা বার করে লোকটার হাতে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে একটা লম্বা সেলাম করলে লোকটা কান্তকে। বললে—চলো–
লোকটার পেছন পেছন কান্ত এগিয়ে যেতে লাগল আর একটা ইট-বাঁধানো রাস্তা দিয়ে।
.
কিন্তু যতই ভেতরে যেতে লাগল ততই অবাক হবার পালা কান্তর। ভেতরে তখন বোধহয় খুব গোলমাল চলছে। কারা বোরখা পরে সামনের দিকে আসছিল। লোকটার পেছনে দাঁড়িয়ে কান্ত তাদের পথ করে দিলে। আবার পেছন থেকেই দৌড়োতে দৌড়োতে দু’জন লোক আসছিল। তারা চেঁচাতে লাগল–ফিরিঙ্গিলোগ আ গয়া।
কে এসেছে?
কলকাতা-কুঠির টুপিওয়ালা সাহেবলোগ!
কথাগুলো যেন বিদ্যুতের মতো ক্রিয়া করল চারদিকে। কোথা থেকে আর এক দল লোক বেরিয়ে আসতে লাগল পিলপিল করে। তাদের কথাবার্তা থেকে কিছু বোঝা গেল না।
*
কিন্তু কান্ত জানতেও পারলে না মুর্শিদাবাদের গঙ্গার এ-পারে তখন মানুষের ভিড়ে কোথাও তিল ধরবার জায়গা নেই আর। সারা দেশ ঝেটিয়ে মানুষ এসেছে ইতিহাসের আর এক মজা দেখতে। এতদিন যারা। ঘরের হুড়কো এঁটে মুখে কুলুপ লাগিয়ে বসে ছিল, তারা সবাই গঙ্গার ঘাটে এসে ভিড় জমিয়েছে। এসেছে! ফিরিঙ্গি-কোম্পানির সাহেবরা এসেছে। আর ভয় নেই। এবার ঘরের মেয়েছেলে নিয়ে। নিশ্চিন্তে গেরস্থালি করব। জোর করে কেউ কলমা পড়াবে না। একসঙ্গে দূর থেকে পালতোলা ক’টা জাহাজ বেশ গম্ভীর চালে এগিয়ে আসতে লাগল। মুর্শিদাবাদের মানুষ আনন্দে লাফিয়ে উঠল সেই দিকে। চেয়ে। কাউকে চিনতে পারবার জো নেই। লাল-লাল মুখ সব। গোরা পল্টন। সবসুদ্ধ গোটা তিরিশেক। লোক হবে, তার বেশি নয়।
ক্লাইভ সাহেবের কেমন ভয় করতে লাগল। সবাই যদি একটা করে ঢিল ছুঁড়ে মারে তা হলেই তো আর তাদের দেখতে হবে না। পাশেই গভর্নর ড্রেক সাহেব। মেজর কিলপ্যাট্রিক, মেজর গ্র্যান্ট, মিস্টার ম্যানিংহাম, অমিয়ট, স্ক্র্যাফটন, ওয়াটসন। আর পেয়ারের মুনশি নবকৃষ্ণ। আরও অনেকে। সামনের ফৌজিদল আস্তে আস্তে শহরে ঢোকবার চেষ্টা করতে লাগল। আর সঙ্গে সঙ্গে মুর্শিদাবাদের মানুষ শাখ বাজাতে, উলু দিতে লাগল।
কান্ত দেখে, ক্লাইভ সাহেব পাশে দাঁড়ানো মিরজাফর আলিকে জিজ্ঞেস করলেওরা কী বলছে? ওরা কারা? ও কীসের সাউন্ড?
মিরজাফর বললে–ও কিছু না কর্নেল, ওরা সবাই হিন্দু, আপনারা আসছেন শুনে ওদের খুবই আনন্দ হয়েছে, আনন্দ হলেই ওরা ওইরকম চিল্লাচিল্লি করে–
তখন সবাই আরও সামনে এগিয়ে এল। আরও জোরে শাঁখ বেজে উঠল। আরও জোরে উলু দিতে লাগল মুর্শিদাবাদের মানুষেরা। উ-লু-লু-লু-লু-লু—
.
সেইখানে সেই নিজামত-হারেমের সামনে দাঁড়িয়েই কান্ত যেন আর এক পৃথিবীতে পৌঁছে গেছে। ছোটবেলা থেকে বড় হওয়ার বৈচিত্র্য দেখতে দেখতে আর অনুভব করতে করতে বিচিত্ৰতর এক জগতের মধ্যে যেন সে ঢুকে পড়েছে। সেই বড়চাতরা, সেই চৌধুরীদের চকমিলানো বাড়ি আর সেই বগি। সে যেন তার অতীত। সেই অতীতটার ভিতের ওপর তার ভবিষ্যতের সৌধ গড়তে গিয়ে দেখেছিল, কলকাতার বেভারিজ সাহেবের সোরার গদিবাড়িটা বেশ মজবুত করে গেঁথে তুলেছে সে। সেটা যখন ভেঙে গেল, তখন আর নতুন করে গড়বার কিছু ছিল না তার। সেও ওই হাতিয়াগড়। হাতিয়াগড়ের একটা বাড়িতে গিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসবার স্বপ্নও দেখেছিল সে। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেই কি সবকিছু হয় না সবকিছু থাকলেই ইচ্ছে হয়। আসল ইচ্ছের সঙ্গে ইচ্ছেপূরণের কোনও সম্পর্কই নেই।
হাতিয়াগড়ের রানিবিবি সেই কথাই জিজ্ঞেস করছিল কাটোয়াতে।
.
সবই যদি ঠিক ছিল তো বিয়ে হল না কেন?
কান্ত বলেছিল–আমার যে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল যেতে
রানিবিবি অবাক হয়ে বলেছিল–সেকী? মানুষের খেতে দেরি হতে পারে, ঘুমোতে যেতেও দেরি হতে পারে, কিন্তু তা বলে তুমি বিয়ে করতে যেতেই দেরি করে ফেললে? ঘুমিয়ে পড়েছিলে বুঝি?
কান্ত লজ্জায় পড়ল। রানিবিবি যে তার সঙ্গে এমন কথা বলবেন, তা সে কল্পনাও করতে পারেনি। রানিবিবির মুখখানা একেবারে খোলা। মানে তার মতো অচেনা পুরুষমানুষের সঙ্গে দেখা করতে এতটুকু সংকোচও নেই। আর তা ছাড়া রানিবিবির বয়েসটা যে এত কম হবে, তাও তো ভাবতে পারেনি সে। বেশ জ্বলজ্বলে টাটকা সিঁদুর রয়েছে মাথার সিথিতে। সকালবেলা স্নান করে চুল এলো করে দিয়েছে পিঠের দিকে। বাঁদিটা বোধহয় তাম্বুলাবহার দিয়ে পান সেজে দিয়েছিল, তাই চিবোচ্ছে।
আপনার খাওয়ার কোনও অসুবিধে হয়নি তো? আমি কোতোয়ালিতে আপনার খাওয়ার কথা বলতে গিয়েছিলাম। শেষকালে হয়তো গোস্তটোত খাইয়ে দেবে, এই ভয় করছিলুম–
আমি গোস্ত খাই তো!
সেকী, আপনি গোরুর মাংস খান?
হেসে উঠল রানিবিবি–মোগলের হাতে যখন পড়েছি, তখন গোরুর মাংস খাওয়ালেই বা কী, আর শুয়োরের মাংস খাওয়ালেই বা কী! ওকথা থাক, তোমার বিয়ের কথাটা বলো—
কান্ত লজ্জায় পড়ল। বললে–কপালে আমার বিয়ে না থাকলে কী হবে!
দোষটা করলে তুমি নিজে আর নিন্দে করছ কপালের!
কিন্তু আপনি তো জানেন না, ফিরিঙ্গি কোম্পানির চাকরি কী জিনিস। কোথায় সেই সুতোনুটি আর কোথায় সেই হাতিয়াগড়। বেভারিজ সাহেবের সোরার নৌকো এল দেরি করে, সেই নৌকোর সব মাল খালাস করে গুদামে পুরে হিসেব না করলে তো ছুটি নেই। তারপরে যে-নৌকোয় করে হাতিয়াগড়ে যাবার বন্দোবস্ত করেছিলাম, তা মাঝপথে চড়ায় আটকে গেল আর বিয়ের লগ্ন ছিল রাত দু’প্রহরের সময়–
শেষপর্যন্ত কী হল?
কান্ত বলল–ভেবেছিলাম আমার জন্যে পাত্রীপক্ষ অপেক্ষা করবে, কিন্তু গাঁয়ের লোক তাড়াহুড়া করলে বলে আর একজনকে ধরে এনে তার সঙ্গে সেই লগেই বিয়ে দিয়ে দিয়েছিল পাত্রীর বাপ–
কোথায় বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল?
হাতিয়াগড়ে। আপনাদেরই জমিদারিতে। আপনি হয়তো তাদের চিনবেন। পাত্রীর বাবার নাম শোভারাম বিশ্বাস–
রানিবিবি তাদের চিনলেন কিনা কে জানে। সে-সম্বন্ধে আর কিছু বললেন না। একটু পরে জিজ্ঞেস করলেন–সেই দুঃখেই বুঝি ফিরিঙ্গি কোম্পানির চাকরি ছেড়ে দিয়ে নবাব সরকারে চাকরি নিলে?
না, ঠিক তা নয়, ওখানে তিন টাকা তলব পেতাম, এখানে পাব ছ’ টাকা।
শুধু টাকার লোভেই এই চাকরি নিলে না আর কোনও লোভও ছিল?
আর কী লোভ থাকতে পারে বলুন! জিনিসপত্তরের যা দাম বাড়ছে, তাতে তিন টাকা মাইনেতে আর কুলোচ্ছে না। সেই শায়েস্তা খাঁর আমল কি আর এখন আছে!
সংসারে তোমার কে কে আছেন?
কেউ নেই। শুধু আপনি আর কোপনি।
বলে কান্তও হাসল, আর তার সেই হাসিতে রানিবিবিও হাসল। একবার কান্তর ইচ্ছে হল জিজ্ঞেস করে, মুর্শিদাবাদের নবাব-হারেমে কেন যাচ্ছেন রানিবিবি। কিন্তু কথাটা কেমন করে পাড়বে, সেই ভাবতে গিয়েই আর বলা হল না। তারপর নিজেই একটা কারণ অনুমান করে নিয়ে বললে–আপনি হয়তো ভাবছেন, আমি এর মধ্যে আছি–
কীসের মধ্যে?
এই আপনাকে নবাব-হারেমে নিয়ে যাবার মধ্যে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি এর কিছুই জানিনে। বরং আমি বশিরকে জিজ্ঞেস করেছিলুম–
বশির কে?
নিজামত কাছারিতে মোহরার মনসুর আলি মেহের খাঁ সাহেব আছেন, তার সম্বন্ধীর ছেলে। সে আমার বন্ধু। তাকে অনেকবার জিজ্ঞেস করেছিলুম, কিন্তু সে কিছু বললে–না। আমি শুধু হুকুম তামিল করছি। এই পাঞ্জা দিয়েছে আমাকে ওরা। বলেছে, এটা দেখালে রাস্তার সেপাই কি ফৌজদারের লোক কেউ কিছু বলবে না–আপনি হয়তো মনে মনে আমাকে দুষছেন।
কেন, তোমাকে দুষতে যাব কেন?
জানি না, হয়তো আপনাকে এইরকম করে নিয়ে গিয়ে আপনার কোনও ক্ষতি করছি। সত্যি বলুন তো, আপনি একা একা সেখানে যাচ্ছেন কেন? আপনার কি কিছু কাজ আছে?
রানিবিবি একবার একটু গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর আর-একটা পান মুখে পুরে দিয়ে বললে–এ কথার উত্তর যদি দিই, তা হলে তোমার চাকরিটাই চলে যেতে পারে। আমার কিছু হলে তোমার কিছু যাবে-আসবে না, কিন্তু তোমার চাকরি চলে গেলে তখন কী করবে?
কান্ত এবার রানিবিবির মুখের দিকে সোজাসুজি চেয়ে দেখলে। যেন কথাগুলোর মানে খোঁজবার চেষ্টা করলে রানিবিবির মুখ-চোখ-ঠোঁটের মধ্যে।
রানিবিবি আবার বলতে লাগল–দিনকাল খারাপ, এসময়ে দুটো টাকা যেখান থেকে পায়রা জোগাড় করে জমাতে চেষ্টা করো। টাকাটাই এখন সব আখেরে টাকাই কাজ দেবে!
কেন? ওকথা বলছেন কেন?
দেখছ না, নবাব থেকে শুরু করে সেপাই পর্যন্ত সবাই টাকা টাকা করে মরছে। টাকার জন্যেই তো ফিরিঙ্গিরা সাত-সমুদ্র পেরিয়ে এখানে এসেছে। বর্গিরাও তো টাকার জন্যে আসত এখানে
আপনি বুঝি আমাকে ঠাট্টা করছেন?
ঠাট্টা করব কেন? তুমি নিজেই তো টাকার জন্যে একটা মেয়ের জীবন নষ্ট করলে। টাকাটাই কি সব নয়?
কান্ত অবাক হয়ে গেল।–আর আপনি? আপনিও কি তাই টাকার জন্যে মুর্শিদাবাদ যাচ্ছেন?
আমি কী জন্যে যাচ্ছি, তা তোমাকে বলতে যাব কেন? আর যার জন্যেই যাই, টাকার জন্যে নিশ্চয়ই। নয়। তা ছাড়া, মেয়েমানুষরা অত টাকা-টাকা করে না। বিয়ে হলে তুমি বুঝতে পারতে–
কান্ত বললে–কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন, আমার বিয়ে করবার খুব ইচ্ছে ছিল, ভেবেছিলাম বিয়ে করে বড়চাতরায় নিয়ে যাব আমার বউকে, সেখানকার বাড়িটা সারিয়ে সুরিয়ে সেখানেই সংসার করব, ভেবেছিলাম বর্গি আসা যখন বন্ধ হয়েছে তখন আবার দেশে গিয়ে চাষবাস করব। সত্যি আমার এসব ভাল লাগছে না।
তারপর রানিবিবির দিকে চেয়ে হঠাৎ কথা বলতে বলতে থেমে গেল। বললে–আপনাকে আমার নিজের এত কথা বলছি বলে আপনি বিরক্ত হচ্ছেন না তো?
বিরক্ত হব কেন, বলো না।
বলে হাসলেন রানিবিবি।
সত্যি, কান্ত জীবনে এই প্রথম যেন একজন শ্রোতা পেয়েছে। তার অনেক কথা অনেকদিন ধরে বুকের মধ্যে জমে ছিল, শোনবার লোকই কেউ ছিল না। বেভারিজ সাহেবের সোরার গুদামে কেবল মালের হিসেবই রেখেছে সারাদিন ধরে। তারপর গঙ্গার ধারে খড়ের চালাটায় শুতে-না-শুতে এক ঘুমে। রাত কাটিয়ে দিয়েছে। কোনও কিছু ভাববার সময়ই ছিল না তখন। কিন্তু এক-একদিন যখন কালবোশেখীর ঝড় উঠত, ঝড়ে সোরার নৌকোগুলো, কোম্পানির জাহাজগুলো জলের ঢেউ লেগে ওলোটপালোট করত, সেইসব রাত্রে নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হত তার। এক-একদিন বেভারিজ সাহেবও মদ খেয়ে বেসামাল হয়ে পড়ত। তখন সাহেবের মালী কোথা থেকে সাহেবকে মেয়েমানুষ এনে জুগিয়ে দিত। কোথা থেকে তাদের আনত সে কে জানে! চাকরি বজায় রাখার জন্যে সব কাজই করতে হত তাকে। তখন মনে হত তারও পাশে একজন কেউ থাকলে ভাল হত। তার মুখে গালে চুলে ঠোঁটে হাত দিয়ে আদর করত সে। তাকে নিয়ে বড়চাতরার সেই ঘরখানার তলায় সংসার পাতত। কিন্তু তারপর আবার কখন রাত পুইয়ে যেত। গঙ্গার ঘাটে আবার নৌকোয় পাল খাটানো হত। ভোরবেলাই নৌকোগুলো ছেড়ে দিত বদর-বদর বলে। তখন আর ওসব কিছু মাথায় আসত না। তখন আবার সোরা, তখন আবার হিসেবের খাতা, তখন আবার মোহর-টাকা-কড়া-ক্রান্তির গোলকধাঁধার মধ্যে ডুবে যেত।
তা সেই সময়েই একদিন এক ঘটকমশাই এসে হাজির। হাতে খেরো বাঁধানো খাতা। সচ্চরিত্র পুরকায়স্থ তার নাম। বেশ ভাল করে কান্তর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে, কুলজিবংশ সবকিছু জেনে নিয়ে বলেছিল–তুমি বিয়ে করবে বাবাজীবন?
আসলে ওইভাবেই শুরু হয়েছিল সম্বন্ধটা। হাতিয়াগড়ের সৎকায়স্থ শোভারাম বিশ্বাস। তার একমাত্র সন্তান। মেয়েটিকে পাত্রস্থ করতে চায় তার বাপ। জমিদারি-সেরেস্তায় কাজ করে সে নিজে। নিজের বাস্তুভিটে আছে হাতিয়াগড়ে। দেবেথোবে ভাল। পৈতৃক সোনাদানা কিছু আছে। জামাই-ই সরকিছু পাবে।
কথা বলতে বলতে কান্ত থামল। বললে–এসব কথা আপনার শুনতে হয়তো ভাল লাগছে না—
না না, বলো! তারপর? পাত্রী কেমন দেখতে?
কান্ত বললে–সে কথাও জিজ্ঞেস করেছিলুম—
ঘটকমশাই কী বলেছিলেন? দেখতে খারাপ?
না, ঘটকমশাই বলেছিলেন পাত্রী খুব সুন্দরী।
খুব সুন্দরী?
কান্ত বললে–হ্যাঁ, খুব নাকি সুন্দরী, অমন সুন্দরী নাকি দেখা যায় না—
কার মতন সুন্দরী?
কান্ত বললে–তা জানিনে, আমি তো নিজের চোখে পাত্রী দেখিনি—
তবু শুনে কেমন মনে হয়েছিল? আমার চেয়েও সুন্দরী?
রানিবিবি যে কতখানি সুন্দরী তা যেন এতক্ষণ দেখবার সুযোগ পায়নি। তাই ভাল করে আর একবার রানিবিবির মুখখানা দেখলে সত্যিই এমন সুন্দরী হয় নাকি কেউ!
কান্ত বললে–আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন—
ওমা, ঠাট্টা করব কেন? আমার চেয়ে সুন্দরী কেউ হয় না?
কান্ত বললে–আপনার চেয়ে সুন্দরী আবার হয় নাকি? আমি তো জীবনে দেখিনি—
রানিবিবি এবার আবার একটা পান মুখে পুরল। বলল–বেশি সুন্দরী হলে কপালে সুখ হয় না, তা জানো তো?
কেন? আপনার কি সুখ হয়নি?
রানিবিবি কী একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই হঠাৎ বাইরে যেন কার গানের আওয়াজ হল। বাইরের গাছতলায় যেখানে সেপাইরা বসে ছিল, সেইখান থেকেই গানের শব্দটা আসছিল। রানিবিবি মন দিয়ে সেই গানটা শুনতে লাগল। কান্তও শুনতে লাগল। গানটা নতুন।
কোথায় শিবে, রাখো জীবে, ত্রৈলক্য-তারিণী।
তোমার চরণ নিলাম শরণ বিপদ-হারিণী ॥
আমি মা অতি দীন।
আমি মা অতি দীন তনু ক্ষীণ, হলো দশার শেষ
কোন দিন মা রবি সুতে ধরবে এসে কেশ ॥
লোকে গান শুনছে আর তারিফ করছে। বলছে–বাঃ বাঃ বলিহারি–বলিহারি—
কে একজন বললে–ও-গান নয় হে, এবার একটা প্রেমসংগীত গাও তো হে—
লোকটা বললে–একটা খেদের গান গাই শুনুন হুজুর—
তাই গাও—
আবার গান হতে লাগল–
আমি রব না ভব-ভবনে–
শুন হে শিব শ্রবণে ॥
যে নারী করে নাথ হৃদিপদ্মে পদাঘাত
তুমি তারই বশীভূত আমি তা সব কেমনে ॥
রানিবিবি হঠাৎ যেন গম্ভীর হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করলে–ও কে গাইছে ওখানে?
কান্ত বললে–কী জানি, আপনিও যেখানে আমিও সেখানে গানটা থামাতে বলে আসব?
রানিবিবি বললে–না, তুমি জেনে এসো তো লোকটা কে, ওর নাম কী?
কেন, আপনি চেনেন নাকি ওকে?
তুমি জেনেই এসো না—
কান্ত বাইরে যাচ্ছিল, পেছন থেকে রানিবিবি আবার মনে করিয়ে দিলে–নামটা জেনে এসে আমাকে বলবে কিন্তু–
বাইরে তখনও গান হচ্ছে
পতিবক্ষে পদ হানি ও হল না কলঙ্কিনী
মন্দ হল মন্দাকিনী ভক্ত হরিদাস ভনে।
আমি রব না ভব-ভবনে।
তখন গানটা আরও জমে উঠেছে। অশ্বথ গাছতলাটার নীচেয় বেশ গুছিয়ে বসেছে সেপাইরা। আর মধ্যিখানে একটা আধাবয়সি লোক হাত-মুখ নেড়ে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে গান গাইছে। কান্ত সামনে আসতেও যেন লোকটার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। খানিক পরে গান থামিয়ে লোকটা কান্তর দিকে চাইল।
তোমার নাম কী গো?
লোকটা রসিক খুব। বললে–আমি হরির দাস হুজুর, আমার আবার নাম কী! তাঁর নাম গান করেই তো বেঁচে আছি–
তবু নাম তো একটা আছে, বাপ-মায়ের দেওয়া নাম, আমাদের রানিবিবি জানতে চাইছেন—
রানিবিবি!
রানিবিবির নাম শুনে লোকটার বোধহয় একটু চেতনা হল। বললে–ভেতরে বুঝি রানিবিবিকে নিয়ে লীলেখেলা হচ্ছে? তা ভাল, তা ভাল–আমার নাম উদ্ধব দাস; রানিবিবিকে গিয়ে বলো–
তারপর কথাটা বলেই লোকটা আর একটা গান ধরতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই কোতোয়াল এসে হাজির। কোতোয়ালকে দেখে সেপাই টেপাই যারা ছিল সবাই সসম্ভ্রমে পঁড়িয়ে উঠল।
তুমি আবার এখানে?
বন্দেগি হুজুর, আমি হরির দাস, ভক্ত হরিদাস–আমি আর যাব কোথায় বলুন–অধীনের কি আর যাবার জায়গা আছে?
কথাটা শেষ হবার আগেই কোতোয়াল বললে–ভাগো এখান থেকে, ভাগো–
বলে আর সেদিকে না-চেয়ে সেপাইদের দিকে চাইলে। কান্তকেও একবার দেখলে। তারপর হুকুম হল তখনই রওনা দিতে হবে মুর্শিদাবাদের দিকে। কোতোয়াল সাহেব গম্ভীর স্বভাবের মানুষ। একেবারে যে-কথা সেই কাজ। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পালকিতে ঘেরাটোপ লাগিয়ে দিয়ে সকলকে রওনা করিয়ে দিয়েছিল। আবার পালকি চলতে লাগল রানিবিবিকে নিয়ে। রানিবিবির সঙ্গে তার কথাই হল না, দেখা তো দূরের কথা। শুধু দূর থেকে ভক্ত হরিদাসের গানের কথাগুলো একটু একটু ভেসে আসছে–
পতিবক্ষে পদ হানি ও হল না কলঙ্কিনী
মন্দ হল মন্দাকিনী ভক্ত হরিদাস ভনে।
আমি রব না ভব-ভবনে।
উদ্ধব দাসকে বুঝি ভব-ভবনে রাখাই যায় না। উদ্ধব দাস তাই কেবল এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। গান গায় আর ঘুরে বেড়ায়। রানিবিবির পালকির পেছন পেছন চলতে চলতে কান্ত তখনও কেবল কথাটা ভাবছিল। খানিকক্ষণের জন্যে দেখা। অনেক কথা জানতে চেয়েছিলেন। কান্তর জীবনের। কান্তর কথা বড় মন দিয়ে শুনেছিলেন রানিবিবি। সকলে কি সকলের কথা শোনে নাকি! বিশেষ করে কান্ত তো তার পর। কান্তর দুঃখের কথা শুনে লাভই বা কী হত তারা বলেছিলেন–নামটা জেনে এসে আমাকে বলবে। অথচ বলা হল না। পুরনো সেপাই বদল হয়ে গেছে। এবার কাটোয়ার কোতোয়ালের নতুন সেপাই চলেছে সঙ্গে।
*
চেহেল্-সুতুনের ভেতরে বোরখায় মুখ ঢেকে সব কথাগুলোই মনে পড়ছিল। অথচ এই তো সেদিন। সবে সঙ্গে করে এনেছে রানিবিবিকে, তারই মধ্যে সমস্ত ওলোট পালোট হয়ে গেল। তারই মধ্যে লড়াই। শুরু হল, লড়াই শেষও হয়ে গেল। মসনদ পর্যন্ত বদলি হব হব। কে নবাব হবে কে জানে! এখন তলবটা পেলে হয় শেষপর্যন্ত! কান্ত সেই অল্প-অল্প আলো-ছায়ার ভেতর দিয়ে রানিবিবির কথাই ভাবতে লাগল। কোথায় সেই কাটোয়া আর কোথায় এই মুর্শিদাবাদ। এই পথ দিয়ে কত নবাব কত বেগম ভেতরে এসেছে, আবার ভেতর থেকে বাইরেও গিয়েছে। এই পথ দিয়েই মুর্শিদকুলি খাঁ এসেছে একদিন এইখানে। এইখানে দাঁড়িয়েই রাজবল্লভ সেন ঘসেটি বেগমের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছে। কাটোয়ায় ভাস্কর পণ্ডিতকে খুন করে এইখান দিয়েই আলিবর্দি খাঁ এই হারেমে ঢুকেছে। দেখতে দেখতে কান্তর চোখের সামনে দিদিমার কাছে শোনা গল্পগুলো যেন আবার দেখতে পেল। আবার ঘনিয়ে এল সেই সব রাত, সেই সব দিন, সেই সব কাল। একদিনের মধ্যে সব ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেল। মনে হল এখনও যেন এখানে-ওখানে নবাবের রক্ত লেগে রয়েছে। কোথায় গেল সেই হোসেন কুলি খাঁ, কোথায় গেল সেই আলিবর্দি খাঁ। ইতিহাসের পাখায় চড়ে যেন সবাই আবার ফিরে আসতে লাগল উড়ে উড়ে। দিদিমা সব জানত। দিদিমার কথাই যেন সত্যি হল। যেন পায়ের তলার শব মাড়িয়ে সে ইতিহাসের সিংহদ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে আজ। আজ যদি মসনদই নেই, আজ যার জন্যে এখানে রানিবিবিকে আনা সেই নবাবই যখন নেই, তখন কেন রানিবিবি এখানে থাকবে? কোথাকার কোন খোরাসান, কান্দাহার, চট্টগ্রাম থেকে। আনা বেগমরা যেন এতদিন পরে ইতিহাসের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেয়েছে। একসঙ্গে সবাই বুঝি তাই হেসে উঠেছে। মুক্তির হাসি, আনন্দের হাসি, স্বাচ্ছন্দ্যের হাসি। কান্ত সেইখানে বসেই ইতিহাসের অমোঘ বাণী যেন শুনতে লাগল।
মরিয়ম বেগম, মরিয়ম বেগম!
বাইরের ডাকে যেন হঠাৎ কান্তর সংবিৎ ফিরে এল। কে যেন দরজা ঠেলছে আর ডাকছে–মরিয়ম বেগম, মরিয়ম বেগম—
*
জেনারেল ক্লাইভ ডাকলে—মুনশি–
মুনশিকে সঙ্গেই এনেছিল ক্লাইভ সাহেব। টিকি দোলাতে দোলাতে মুনশি নবকৃষ্ণ সামনে এসে হাজির।
হুজুর!
বশির দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল একপাশে। মনসুর আলি মেহেরও দাঁড়িয়ে ছিল। মিরজাফর খাঁ দাঁড়িয়ে ছিল। জামাই মিরকাশিম খাঁ-ও দাঁড়িয়ে ছিল। ছেলে মিরন দাঁড়িয়ে ছিল। নিজামত সরকারের আমলা-ওমরাহ সবাই হাজির। সারা মুর্শিদাবাদের নোক আজ শহর-গ্রাম-জনপদ ঝেটিয়ে এসে মুর্শিদাবাদের নবাবের আম-দরবারে হাজির। সবাই ভেতরে ঢুকতে পারেনি। সবাইকে চুকতে দেওয়া হয়ওনি। এত মানুষ দেখে কর্নেল সাহেবের লাল চোখ-মুখ আরও লাল হয়ে গেছে। সকাল থেকেই করোরিয়ান, চৌধুরীয়ান, জমিদারানরা হাজির ছিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গোড়া থেকেই সামনে ছিলেন। যা-কিছু নবাবের মালখানার সিন্দুক থেকে পাওয়া গিয়েছে সব জড়ো করে তুলে নিয়েছে ক্লাইভ সাহেব। এত মোহর, এত টাকা, এত হিরে, এত চুনি, এত পান্না, এত কিছু জীবনে দেখেনি সাহেব। প্রথমে সিন্দুকটা খুলতেই চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল সাহেবের। মুনশি নবকৃষ্ণ পাশেই ছিল। তারও চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। শায়েস্তা খাঁ শুধু নয়। বখতিয়ার খিলিজির আমল থেকেই এই টাকা জমে জমে পাহাড় হয়ে উঠেছিল মুর্শিদাবাদের খাজাঞ্চিখানায়। মুর্শিদকুলি খাঁ’র সময় থেকেই আরও পাকাপাকি রকমের জমা বন্দোবস্ত হতে শুরু করেছিল। তার বন্দোবস্তের নাম ছিল জমা কাসেল তুমারি। সারা বাংলাদেশের টাকা এসে ঢুকত এইসব সিন্দুকে। এসে পুরুষানুক্রমে জমা হয়েছে এখানে। সে-টাকা দেখে চোখ ঘুরে যাবার মতো অবস্থা হল কর্নেলের।
মুনশি নবকৃষ্ণ বললে–এ-সব আপনার হুজুর–আপনি নিন—
কর্নেল সাহেব যা নিলে তা নিলে। তারপর নিলে মুনশি।
আমি যে সঙ্গে কিছু বাক্সটাক্স আনিনি।
আমি সিন্দুকসুষ্ঠু আপনাকে দেব, আপনার নিতে কোনও অসুবিধে হবে না–একেবারে জাহাজে তুলে সুতানুটিতে পাঠিয়ে দেব আপনার হাবেলিতে–
মাসিক সাত টাকা মাইনের চাকরিতে ঢুকে এখানে এসেছিল ক্লাইভ সাহেব। সঙ্গে সঙ্গে রাজত্ব পাওয়া হয়ে গেল। কিন্তু শুধু রাজত্ব তো দেওয়া যায় না। রাজকন্যা দেওয়ারও নিয়ম আছে এ-দেশে। মিরজাফর খাঁ তাও দিলেন। রাজকন্যা নয়, নবাব-বেগম।
ক্লাইভ মুশকিলে পড়লে। বললে–এদের নিয়ে আমি কী করব?
হুজুর, এইটেই যে কানুন। নবাবের যা কিছু আছে সবই আপনার। নবাবের টাকা আপনাকে দিয়েছি, নবাবের এই বেগমদেরও আপনাকে নিতে হবে–
বলে ডাক পাড়ল–নুর বেগম–
সমস্ত বন্দোবস্ত আগে থেকেই করা ছিল। হারেমের খোঁজা-সর্দার পিরালিকে আগে থেকেই হুকুম দেওয়া ছিল। সমস্ত বেগমরা সকাল থেকেই সাজতে গুজতে শুরু করেছে। চোখে সুরমা দিয়েছে, বুকে বুটিদার কঁচুলি পরেছে, ঠোঁটে আলতা মেখেছে, নখে মেহেদি রং লাগিয়েছে; ঘাগরা, চোলি, ওড়নি কিছুই বাদ যায়নি। আজ সবাই হারেম ছেড়ে আর-এক হারেমে গিয়ে উঠবে। এতদিন যাকে মনোরঞ্জন করবার জন্যে তারা জন্মেছিল, সে নেই। এবার অন্য একজনের মনোরঞ্জন করবার জন্যে আবার বেঁচে থাকতে হবে। আবার বিকেল থেকে প্রতিদিন আর একজনের মন ভোলাবার জন্যে তৈরি হতে হবে। সে দিশি নবাব নয়, সে সাহেব। লাল পল্টনদের গোরা সাহেব। লক্কাবাগের লড়াইতে যে-সাহেব নবাবকে হারিয়ে দিয়েছে।
জিন্নৎ বেগম!
আজ আর কারও কোনও অভিযোগ নেই। অবশ্য অভিযোগ ছিলও না কোনওদিন। নবাব হারেমে কোনও অভিযোগ থাকতে নেই কারও। খেতে পরতে পেরেছে একদিন, আবার এবার যেখানে যাবে সেখানেও তারা খেতে পরতে দেবে। আমরা জারিয়া। মানে ক্রীতদাসী। আমাদের আবার জাতকুল কী, আমাদের আবার মান-সম্মান বা কী।
তক্কি বেগম।
এক-একজনের নাম ডাকা হয় আর সে ওড়নি ঢাকা দিয়ে মাথা নিচু করে এসে দাঁড়ায়। একজনের পর আর একজন। তারপর আর একজন। আম-দরবারের শোভা যেন আজ হাজার গুণ বেড়ে গেছে রূপসিদের জেল্লার জৌলুসে! রসুননচৌকিতে এতক্ষণ মিঞা-কী মল্লার বাজাচ্ছিল নবাব নিজামতের বহুদিনের মাইনে-করা পুরনো নহবতি বুড়ো ইনসাফ মিঞা। সে এ-রাগ বহুবার আগে বাজিয়েছে। বুড়ো নবাবসাহেব যেবার কাটোয়াতে বর্গিসর্দার ভাস্কর পণ্ডিতকে খুন করে রাজধানীতে ফিরে এসেছিলেন, সেবারও ইনসাফ মিঞা এই মিঞা-কি-মল্লারই বাজিয়েছিল। যেবার বুড়ো নবাবের নাতি মির্জা মহম্মদের বিয়ে হল সেবারও একবার বাজিয়েছিল এই মিঞা-কি-মল্লার। বড় কড়া রাগ। তানসেনজির নিজের মেজাজের তৈরি জিনিস। তানসেনজি বাদশা আকবর শাহকে এই মিঞা-কি-মল্লার পেশ করেছিলেন। এ-রাগ যখন-তখন যাকে-তাকে শোনানো যায় না।
তাড়াতাড়ি বশির মিঞা দৌড়ে এসেছে রসুনচৌকির ওপরে।
এ কী বাজাচ্ছ মিঞাসায়েব?
কেন জনাব, এ তো মিঞা-কি-মল্লার!
না না, গোরা সাহেবরা ওসব বুঝতে পারবে না। নবাবসাহেব গোসা করছেন—
নবাব? কোন নবাব?
নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা যে নেই তা যেন জানে না ইনসাফ মিঞা। তা যেন শোনেইনি সে। বচপন থেকে মির্জাকে দেখে এসেছে ইনসাফ মিঞা। মির্জা মহম্মদ সেই ছোটবেলাতেই এই নহবতখানায় উঠে এসে বাঁশির ফুটোতে ফুঁ দিতে চেষ্টা করত কতবার। কতবার ইনসাফের চোখের আড়াল থেকে বাঁশি চুরি করে পালিয়েছে। সেই মির্জা মহম্মদই বড় হয়ে তোমাদের সিরাজ-উ-দ্দৌলা হল। তোমরা তার জন্যে না-কাঁদতে পারো, কিন্তু আমি কী করে কান্না থামাই? আমার কি মন কেমনও করতে নেই?
সত্যিই কেউ কাঁদছে না। গোরা সাহেবরা এসেছে বলে মুর্শিদাবাদে যেন মহফিল শুরু হয়ে গিয়েছে। গোরা সাহেবদের জন্যে খানাপিনার বন্দোবস্ত হচ্ছে। সরাবের বন্দোবস্ত হয়েছে। মুরগি-মসল্লমের বন্দোবস্ত হয়েছে। পোলাউ-বিরিয়ানির বন্দোবস্ত হয়েছে। ঠিক মির্জা মহম্মদের বিয়ের সময় যা-যা যেমন-যেমন বন্দোবস্ত হয়েছিল, সব ঠিক তেমনি-তেমনি বন্দোবস্ত হয়েছে। আমি মিঞা-কি-মল্লার বাজাব না তো কি মালগুঞ্জ বাজাব? হোলি বাজাব? খেমটা বাজাব?
গুলসন বেগম!
পেশমন বেগম!
আখতার বেগম!
মুর্শিদাবাদের গ্রামের মানুষ হাঁ করে চেয়ে দেখছিল। এত বেগম একসঙ্গে দেখবার কখনও মওকা মেলেনি তাদের। সমস্ত বেগমই আসবে নাকি রে বাবা! এ তো রূপ নয়, আগুন। আগুনের ডেলা সব পঁড়িয়ে রয়েছে মেয়েমানুষের চেহারা নিয়ে।
ক্লাইভ সাহেব চুপি চুপি মুনশিকে জিজ্ঞেস করলে–এসব ওম্যান কোত্থেকে এসেছে মুনশি?
কেউ এসেছে খোরাসান, কেউ এসেছে কান্দাহার, কেউ এসেছে চট্টগ্রাম থেকে। যেখান থেকে নারী-রত্ন পেয়েছে কুড়িয়ে এনেছিল নবাব।
সমস্ত নিজের ওআইফ?
নবকৃষ্ণ মুনশি বললে–না হুজুর, সব ব্যাডওম্যান, খারাপ মেয়েমানুষ!
মরিয়ম বেগম!
অবাক কাণ্ড! এবার কেউ এল না।
মনসুর আলি মেহের আবার ডাকলে–মরিয়ম বেগম–মরিয়ম বেগম–
এ-ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। এগারোজন বেগম এসে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। আর একজন বাকি আছে। সবসুন্ধু বারোজন বেগম। কিন্তু মরিয়ম বেগম আসছে না কেন? পিরালি তখন হারেমের ভেতরে গোরু-খোঁজা শুরু করে দিয়েছে। এ-ঘরে যায়, ও-ঘরে যায়। কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। সাজিয়ে গুছিয়ে তাকেও তো তৈরি করে রেখে দেওয়া হয়েছিল।
বশির মিঞা দাঁড়াতে পারলে না। কোণের ফটকের কাছে গিয়ে ডাকতে লাগল–পিরালি, পিরালি—
পিরালির তখন প্রাণ যায়-যায় অবস্থা। মরিয়ম বেগমকে কোনও ঘরে পাওয়া যাচ্ছে না। এই তো সেদিন হাতিয়াগড় থেকে নবাবের জন্যে সেখানকার রানিবিবিকে নতুন আমদানি করা হল। নিয়মমাফিক তার নতুন নামও দেওয়া হল–মরিয়ম বেগম! এখন কোথায় গেল!
বশির মিঞা তখনও ডাকছে—পিরালি–
এগারোজন বেগম তখন মাথা নিচু করে ওড়নি ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর বাকি বেগম আসছে। না। কোথায় গেল মরিয়ম বেগম! জেনারেল সাহেবের কাছে বেইজ্জত হয়ে যাবে নাকি মিরজাফর আলি খাঁ সাহেব। নবাব-নিজামতের বদনামি হবে নাকি?
রসুনচৌকিতে ছোটে শাগরেদ হঠাৎ বলে উঠল–চাচা–
ছোটে শাগরেদ সবে নহবতে ফুঁ দিতে শিখছে। ইনসাফ মিঞা বাজাতে বাজাতেই তার চারদিকে চাইলে একবার।
চাচা, মরিয়ম বেগমকে পাওয়া যাচ্ছে না!
পাওয়া যাচ্ছে না!
বলে ইনসাফ মিঞার কী খেয়াল হল কে জানে, সুরটা সমে এসে থামতেই নহবতের মুখটা একবার আঙুল দিয়ে টিপে নিয়ে তখুনি আবার বাজাতে আরম্ভ করল। এবার মিঞা-কি-মল্লার নয়, মালগুঞ্জ। তবলচি সুরের মুখপাতটা শুনেই তবলায় একটা চটি কষিয়ে দিলে–বাহবা ওস্তাদ–বাহবা–
*
পশুপতিবাবু জিজ্ঞেস করলেন–তারপর মশাই? তারপর?
বললাম-পঁড়ান, একটু সবুর করুন! এই একহাজার পাতার পুঁথি কি এত শিগগির শেষ করা যায়? আপনার পূর্বপুরুষ উদ্ধব দাস এক মহাকবি ছিলেন মশাই। গল্প বড় মোচড় দিয়ে দিয়ে বলেন। একটুখানি পড়লেই পরের পাতা পড়বার জন্যে মনটা ছটফট করে–অথচ আসল খুঁটিটা কিছুতেই ছাড়েন না–হাতে রেখে দেন, শেষকালে চালবেন বলে–
সত্যিই উদ্ধব দাস কদিন ধরে একেবারে নেশাগ্রস্ত করে রেখে দিলে। দেখতে পাগলছাগল মানুষ হলে কী হবে, রসের কারবারে একেবারে রসিকরাজ। রসে টইটম্বুর।
পুঁথি যখন পড়া শেষ হল তখন গভীর রাত। সেই কলকাতার মাঝরাত্রেই যেন সমস্ত অষ্টাদশ শতাব্দীটা চোখের সামনে সশরীরে নেমে এল। সেই হাতিয়াগড়ের রানিবিবি, সেই কান্ত, সেই সিরাজ-উ-দ্দৌলা, সেই লক্কাবাগের লড়াই, সেই রবার্ট ক্লাইভ, সেই মহারাজ নবকৃষ্ণ মুনশি, সেই মরিয়ম বেগম আরও কত অসংখ্য চরিত্র চোখের সামনে সব যেন সজীব হয়ে উঠল।
পুঁথি শেষ করে শান্তিপর্বে’ উদ্ধব দাস লিখছেন–
কোম্পানির রাজ্য হইল, মোগল হইল শেষ।
দমদম-হাউসে আইল ইংরেজ নরেশ ॥
কৃষ্ণভজা বৈষ্ণবেরা আতঙ্কেতে মরে।
ব্রাহ্মণ হইয়া হিন্দু যত পইতা ফেলে ডরে ॥
হিন্দু ছিল মুসলিম হইল পরেতে খ্রিস্টান।
এমন দেশেতে বলো থাকে কার বা মান ॥
কোন দেশেতে ঘর বা তোমার কোন দেশে বা বাড়ি।
মরিয়ম বেগম বলে আমি অভাগিনী নারী ॥
পতি থাকতে পতি নাই মোর অনাথিনী অতি।
মনের মানুষ যেখানে থাক আমি তারই সতী ॥
তার যদি বা মৃত্যু ঘটে আমি কীসে বাঁচি।
তারে কাছে লইয়া আইস থাকি কাছাকাছি ॥
বেগম মেরী বিশ্বাসের অমৃত কথন।
ভক্ত হরিদাস ভনে, শোনে সর্বজন ॥