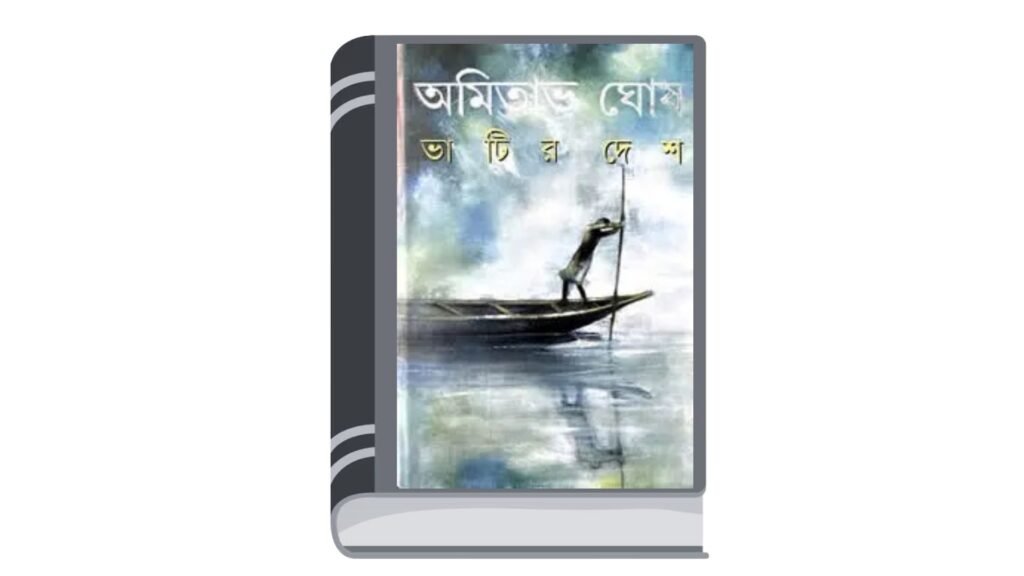২.১ দ্বিতীয় পর্ব – জোয়ার
দ্বিতীয় পর্ব – জোয়ার
পুনরাগমনায় চ
ভেবেছিলাম মরিচঝাঁপির সাময়িক উত্তেজনা আমার চেহারায় যে ছাপ ফেলেছে, লুসিবাড়িতে ফিরতে ফিরতে তা মিলিয়ে যাবে : নদীর হাওয়ায় শরীরও স্নিগ্ধ হবে, আর হরেনের নৌকোর দুলুনিতে ধীর হয়ে আসবে আমার উত্তেজিত হৃৎস্পন্দন। কিন্তু কই? দেখা গেল ঠিক তার উলটোটাই ঘটছে : প্রতিটি বাঁক ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখের সামনে যেন একে একে নতুন সব সম্ভাবনার দরজা খুলে যাচ্ছে। স্থির হয়ে আর বসে থাকতে পারলাম না। ছাতাটা এক ধারে সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালাম, দু’হাত ছড়িয়ে দিলাম দু’দিকে, যেন আলিঙ্গন করতে চলেছি বাতাসকে। হাওয়ার টানে পালের মতো ফুলে উঠল আমার ধুতি, আর আমি দাঁড়িয়ে রইলাম সটান মাস্তুলের মতো–যেন ডিঙিটাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাব দিগন্তের দিকে।
“সার,” চেঁচিয়ে উঠল হরেন, “বসে পড়ুন, বসে পড়ুন। নৌকো কাত হয়ে যাবে যে! একেবারে উলটে পড়বেন জলে।”
“তোমার মতো মাঝি থাকতে নৌকো কখনও উলটোতে পারে হরেন? তুমি ঠিক ভাসিয়ে রাখবে আমাদের।”
“সার, আজ আপনার কী হয়েছে বলুন তো?” হরেন জিজ্ঞেস করল। “আপনাকে আগের মতো তো আর লাগছে না–যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছেন একেবারে।”
“ঠিক বলেছ হরেন। আমি আর সে আমি নেই। একেবারে পালটে গেছি। আর তোমার জন্যই সম্ভব হয়েছে সেটা।”
“কী করে সার?”
“তুমিই তো আমাকে মরিচঝাঁপিতে নিয়ে গেলে, না কি?”
“না সার, ঝড়ে নিয়ে গেল।”
এই রকম বিনয়ী, আমাদের এই হরেন। “ঠিক আছে, ঝড়েই না হয় নিয়ে গেল,” হাসলাম আমি। “এই ঝড়ই তা হলে আমাকে বুঝিয়ে দিল যে রিটায়ার করার পরেও একটা লোকের জীবনে পরিবর্তন আসতে পারে, তার পরেও নতুন করে আবার সব কিছু শুরু করা যায়।”
“কী শুরু করা যায় সার?”
“নতুন জীবন শুরু করা যায় হরেন, নতুন জীবন। এর পর যখন মরিচঝাঁপি যাব আমি, আমার ছাত্ররা সেখানে আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। জীবনে কখনও যে ভাবে পড়ানোর সুযোগ পাইনি, সেইভাবে ওদের পড়াব আমি।”
“কী পড়াবেন সার ওদের? কী শেখাবেন?”
“কেন, আমি ওদের বলব—”
সত্যিই তো, কী বলব আমি ওদের? পাকা মাঝি বটে হরেন, ঠিক হাওয়া কেড়ে নিয়েছে আমার পাল থেকে।
বসে পড়লাম আমি। ভাল করে চিন্তা করা দরকার বিষয়টা নিয়ে।
ঠিক আছে, এই সব ছেলেমেয়েরা যে ধরনের কাল্পনিক কাহিনি-টাহিনির সঙ্গে পরিচিত সেইখান থেকেই শুরু করব আমি। “বল দেখি তোমরা, আমাদের পৌরাণিক গল্পগুলির সাথে ভূগোলের মিল কোথায়?” এরকম ভাবে আরম্ভ করা
যেতে পারে। প্রশ্নটা শুনে নিশ্চয়ই আগ্রহ জাগবে ওদের মনে। চোখ কুঁচকে মিনিট দুয়েক ভাববে, তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করবে–
“কোথায় মিল সার?”
“কেন? দেবদেবীদের কথা ভুলে গেলে?” বিজয়গর্বে পালটা প্রশ্ন করব আমি। “দেবদেবীদের বিষয়টাতেই তো মিল ভুগোল আর পুরাণের।”
ওরা একে অপরের দিকে তাকাবে, ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করবে, “সার কি ঠাট্টা করছেন আমাদের সঙ্গে? মজার কথা বলছেন কিছু?” অবশেষে মিনমিনে দ্বিধাগ্রস্ত গলায় কেউ একজন বলে উঠবে : “কিছু বুঝতে পারছি না তো সার।”
“ভাবো, ভাবো,” বলব আমি। “ভাল করে ভেবে দেখলেই ঠিক বুঝতে পারবে। তখন দেখবে শুধু দেবদেবী কেন, অনেক বিষয়েই মিল আছে পুরাণ আর ভূগোলের মধ্যে। একেকটা পৌরাণিক কাহিনির নায়কদের কথা ভাবো, কী বিশাল তাদের চেহারা–এক দিকে এই সব স্বর্গের দেবদেবীরা, আরেক দিকে এই মাটির পৃথিবীর বিপুল প্রাণস্পন্দন–দুটোই আমাদের কাছে যেন অচেনা, অনেক দূরের কোনও জগৎ। আবার, পুরাণেই বলো কি ভূগোলেই বলো, দেখবে কাহিনিগুলো বা ঘটনাগুলো একের পর এক সব এমনভাবে চলতে থাকে যে প্রতিটা ঘটনারই একটা শুরু আর শেষ থাকে, কিন্তু একটা ঘটনার সঙ্গে পরেরটার একটা যোগ থেকে যায়। একটা কাহিনির শেষ থেকেই গজিয়ে ওঠে আরেকটা কাহিনি। তার পরে ধরো, সময়ের হিসেব–ওদিকে যেমন কলিযুগ, এদিকে তেমনি ভূগঠনের চতুর্থ যুগ। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা খেয়াল করো–এই দুই ক্ষেত্রেই কিন্তু ঘটনাগুলো ঘটছে বিশাল সময় জুড়ে, কিন্তু এমন ভাবে সব কিছু হচ্ছে যে খুব ছোট করেও সেই গল্পগুলি বলে দেওয়া যায়।”
“কী করে, সার, কী করে? এরকম একটা গল্প বলুন না, সার।”
তখন আমি শুরু করব।
বিষ্ণুর উপাখ্যান দিয়েই শুরু করতে পারি। বামনাবতার রূপে কীভাবে মাত্র তিনটি বিশাল পদক্ষেপে গোটা পৃথিবীকে মেপে ফেলেছিলেন বিষ্ণু, সেই কাহিনি শোনাতে পারি। আমি ওদের বলব কেমন ভাবে ভগবানের সেই চলার পথে একবার একটুখানি ভুল পা ফেলার জন্য তাঁর পায়ের একটা লম্বা নখের ছোট্ট একটু আঁচড় লেগে গেল পৃথিবীর গায়ে। সেই আঁচড়ের দাগ থেকেই সৃষ্টি হল আমাদের এই চিরকালের চেনা নদী–যুগ যুগান্ত ধরে যে জগতের সমস্ত পাপ ধুয়ে নিয়ে চলেছে, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নদী–আমাদের এই গঙ্গা।
“গঙ্গা? পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নদী?” আমার কথার মারপ্যাঁচে এত উত্তেজিত হয়ে যাবে ওরা যে আর বসে থাকতে পারবে না। উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে বলবে, “কিন্তু সার, গঙ্গার থেকে লম্বা তো অনেক নদীই আছে : নীলনদ আছে, আমাজন আছে, মিসিসিপি আছে, ইয়াংসিকিয়াং আছে।” তখন আমি বের করব আমার গুপ্তধন, আমার এক ছাত্রের পাঠানো উপহার–সেটা হল ভূতাত্ত্বিকদের বানানো সাগরতলের একটা ম্যাপ। উলটো রিলিফ ম্যাপের মতো সে মানচিত্রে নিজের চোখেই দেখতে পাবে ওরা যে বঙ্গোপসাগরে পৌঁছেই গঙ্গার যাত্রা শেষ হয়ে যায়নি–ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিশে সমুদ্রের নীচে স্পষ্ট এক খাত ধরে আরও বহু দূর বয়ে চলে গেছে। এমনিতে যা জলের তলায় ঢাকা পড়ে থাকে, এই ম্যাপে ওরা তা দেখতে পাবে : দেখতে পাবে মাটির ওপর দিয়ে যতটা পথ গেছে গঙ্গা, তার চেয়ে অনেক দীর্ঘ পথ বয়ে গেছে সমুদ্রের তলার খাত ধরে।
“দেখো, বন্ধুগণ, নিজের চোখেই দেখে নাও,” বলব আমি। “এই ম্যাপে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে পুরাণে যেমন বলা আছে ঠিক তেমনই একটা দৃশ্য গঙ্গা আর একটা লুপ্ত গঙ্গা সত্যি সত্যিই রয়েছে; একটা বয়ে চলেছে মাটির ওপর দিয়ে, আরেকটা বইছে জলের তলা দিয়ে। এবার দুটোকে জুড়ে নাও, তারপর দেখো গঙ্গা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নদী কি না।”
আর তার পরে, আমি ঠিক করলাম, ওদের সেই গ্রিক দেবীর গল্প শোনাব যিনি আমাদের এই গঙ্গার আসল মা। ভূগোলের পথ ধরে বহু বহু যুগ পিছিয়ে নিয়ে যাব ওদের, দেখাব এখন যেখান দিয়ে গঙ্গার ধারা বয়ে চলেছে সেই রেখা এক সময় ছিল উপকূল রেখা–এশীয় ভূখণ্ডের সর্বদক্ষিণ তটভূমি। এই ভারতবর্ষ তখন অনেক অনেক দুরে, অন্য গোলার্ধে। অস্ট্রেলিয়া আর অ্যান্টার্কটিকার সঙ্গে জোড়া ছিল এই দেশ তখন। আমি ওদের দেখাব এশিয়ার দক্ষিণের সেই সমুদ্র, যার নাম ছিল টেথিস। গ্রিক পুরাণ অনুযায়ী টেথিস হলেন ওশেনাসের পত্নী। হিমালয় তখন ছিল না, আর এই সব পুণ্যতোয়া নদী–গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, ব্রহ্মপুত্র তারা তখন কোথায়? আর নদী যেহেতু ছিল না, তাই কোনও ব-দ্বীপও ছিল না। এই বন্যাবিধৌত সমভূমিই বলো, কি পলল মৃত্তিকাই বলো, বা এই বাদাবনই বলো–এসবেরও কোনও চিহ্ন ছিল না। এক কথায়, আমাদের এই বাংলারই কোনও অস্তিত্ব ছিল না তখন। তামিলনাড়ু আর অন্ধ্রপ্রদেশের এই সবুজ তীরভূমি তখন জমাট বরফে ঢাকা, কোনও কোনও জায়গায় সে বরফ পঞ্চাশ থেকে ষাট মিটার পর্যন্ত গভীর। এখন যেটা গঙ্গার দক্ষিণ কূল, সে জায়গা তখন বরফ-জমা এক সাগরতীর–ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে গেছে টেথিস সমুদ্রে, যে সমুদ্রের এখন আর কোনও অস্তিত্ব নেই।
আমি ওদের বলব কেমন করে আজ থেকে চোদ্দো কোটি বছর আগে অস্ট্রেলিয়া আর অ্যান্টার্কটিকা থেকে হঠাৎ ভেঙে বেরিয়ে এসে ভারতবর্ষ শুরু করল তার উত্তরমুখী যাত্রা। ওরা দেখবে কী বেগে ওদের এই উপমহাদেশ এগিয়ে চলেছে, পৃথিবীর অন্য কোনও ভূখণ্ডই কখনও সেই বেগ, অর্জন করতে পারেনি। ওরা দেখবে কীভাবে বিশাল এই ভূভাগের ওজনের চাপে ধীরে ধীরে গজিয়ে উঠছে হিমালয় পর্বত; দেখবে সেই বেড়ে ওঠা পর্বতমালার গায়ে কেমন করে জন্ম নিচ্ছে তিরতিরে একটা ছোট্ট নদী–আমাদের এই গঙ্গা। চোখের সামনে ওরা দেখতে পাবে ভারত যত উত্তরে এগোচ্ছে তত ছোট হয়ে আসছে টেথিস, ক্রমশ সরু হয়ে আসছে মাঝের ফাঁকটুকু। ওরা দেখবে কীভাবে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল সে সমুদ্র কেমন করে দুই ভূখণ্ড মিলে এক হয়ে গেল তাদের সাগর-মায়ের অস্তিত্বের মূল্যে। কিন্তু চোখের সামনে টেথিসের মৃত্যু দেখেও এতটুকু অশ্রুপাত করবে না ওরা, কারণ সঙ্গে সঙ্গে ওদের সামনেই তো জন্ম নেবে দুই নদী, যাদের মধ্যে ধরা থাকবে তার স্মৃতি, জন্ম নেবে টেথিসের দুই যমজ সন্তান–সিন্ধু আর গঙ্গা।
“বলতে পার, কেমন করে বলা যায় যে এক সময় সিন্ধু আর গঙ্গা নদী পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ছিল?”
“কী করে বলা যায় সার?”
“এই শুশুকদের দেখে। এক সময়কার সাগরবাসী এই প্রাণীই হল দুই যমজ নদীর জন্য রেখে যাওয়া টেথিস সমুদ্রের উত্তরাধিকার। সে উত্তরাধিকারকে সযত্নে লালন করেছে এই দুই নদী, আস্তে আস্তে আপন করে নিয়েছে তাকে। সিন্ধু আর গঙ্গা ছাড়া পৃথিবীর আর কোনও নদীতেই এই জাতের শুশুক দেখতে পাওয়া যায় না।”
শুনতে শুনতে যদি দেখি অধৈর্য হয়ে পড়ছে ওরা, তখন এক প্রেমের গল্প বলে আমি শেষ করব আমার কথা। শান্তনু নামের সেই রাজার কথা বলব আমি ওদের, কেমন করে নদীর পাশ দিয়ে যেতে যেতে রাজা একদিন পরমাসুন্দরী একটি মেয়েকে দেখলেন সেই কাহিনি শোনাব আমি। সেই সুন্দরী আর কেউ নন, স্বয়ং গঙ্গা। কিন্তু রাজা সে কথা জানেন না। নদীর পাড়ে এলে যে কোনও স্থিতধী মানুষেরই মাথা ঘুরে যেতে পারে। তো, এই সুন্দরীকে দেখে শান্তনুর খুবই ভাল লেগে গেল, পাগলের মতো তার প্রেমে পড়ে গেলেন তিনি; রাজা প্রতিজ্ঞা করলেন রূপবতী যা চাইবেন তাই তাঁকে দেবেন তিনি, এমনকী তিনি যদি নিজের সন্তানদের জলে ভাসিয়ে দিতে চান তাতেও বাধা দেবেন না।
নদীর তীরে এক রাজার এই মুহূর্তের হৃদয়দৌর্বল্যের কাহিনি থেকে শুরু করেই লেখা হয়ে গেল মহাভারতের গোটা একখানা পর্ব।
সেকালের পুরাণকাররাও যে সত্যকে মেনে নিয়েছিলেন সামান্য এক স্কুলমাস্টার কী করে তাকে অস্বীকার করবে? যে-কোনও নদীতেই আসলে বয়ে চলে ভালবাসার স্রোত। “ছেলেমেয়েরা, এই তা হলে আজকের পড়া। এবার শোনো কবি কী বলেছেন :
“এক কথা, প্রেয়সীকে গান গাওয়া। আর, হায়, অন্য এক কথা
সেই গুপ্ত, অপরাধী শোণিতের দেবতুল্য নদ।”
.
বন্দরের কাল
শুরুতে জলের স্রোত ছিল উলটোদিকে, আর দাঁড় টানছিল ফকির একা, ফলে খুবই ধীরে এগোচ্ছিল নৌকো। প্রায় ঘণ্টাখানেক চলার পর জিপিএস-এ নৌকোর অবস্থান মেপে পিয়া দেখল এতটা সময়ে মাত্র তিন কিলোমিটার এসেছে ওরা। এতক্ষণে হঠাৎ ওর খেয়াল হল ফকিরের কাছে হয়তো বাড়তি এক জোড়া দাঁড় থাকতেও পারে। ইশারায় প্রশ্ন করে বুঝল সত্যিই আছে আর একজোড়া দাঁড়। তক্তার নীচে নৌকোর খোলের মধ্যে রাখা আছে। দাঁড়দুটো। খুশি হয়ে উঠল পিয়া।
দাঁড়গুলোর হালও দেখা গেল ডিঙিটারই মতো, কোনও রকমে জোড়াতালি দিয়ে বানানো। ডালপালা ছাঁটা একজোড়া গাছের ডালের আগার দিকে বেঢপ ভাবে পেরেক দিয়ে আঁটা দুটো কাঠের টুকরো শুধু। ডিঙির কিনারায় পঁড় টানার জন্য কোনও আংটার বালাই নেই, শুধু দুটো খুঁটির ওপর ঠেকা দিয়ে বাইতে হবে। জলের মধ্যে বৈঠা নামাতেই স্রোতের টানে মোচড় খেয়ে গেল সেগুলো। আরেকটু হলেই ভেসে যাচ্ছিল পিয়ার হাত থেকে। হাতের আন্দাজটুকু আসতে খানিকটা সময় লাগল, তবে দু’জনে মিলে দাঁড় টানার ফলে নৌকোর গতি খানিকটা বাড়ল।
কিন্তু যত সময় যেতে লাগল পিয়া দেখল উত্তরোত্তর কঠিন হয়ে উঠছে কাজটা : দুই হাতের তালুতেই বেশ কয়েকটা ফোঁসকা গজিয়ে উঠেছে, মুখে আর ঘাড়ে নুনের আস্তরণ পড়ে গেছে। প্রায় সন্ধে নাগাদ–সূর্য তখন ডুবুডুবু দাঁড় তুলে ফেলল পিয়া। গন্তব্য আর কত দূর সেটা জিজ্ঞেস করার ইচ্ছেটা আর দমন করে রাখতে পারল না। “লুসিবাড়ি?”
সেই সকাল থেকে প্রায় একটানা নৌকো বেয়ে চলেছে ফকির, কিন্তু এখনও ওর চেহারায় কোনও ক্লান্তির ছাপ পড়েনি। পিয়ার প্রশ্ন শুনে মুহূর্তের জন্য থেমে ঘাড় ফিরিয়ে দূরে জলের মধ্যে ঢুকে আসা জিভের মতো একটা চড়ার দিকে ইশারা করল ও। আশেপাশের দ্বীপগুলোর মধ্যে পরিষ্কার, বন জঙ্গলহীন জায়গাটা সহজেই নজরে পড়ছিল। শেষ পর্যন্ত চোখে দেখা যাচ্ছে দ্বীপটা সেটা যথেষ্টই স্বস্তির কথা, কিন্তু বেশ বুঝতে পারছিল পিয়া, ডাঙায় পৌঁছতে আরও অনেকক্ষণ লাগবে ওদের। ঠিকই বুঝেছিল।
নৌকো পাড়ে ভেড়ার পর অবশেষে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে যখন নেমে এল ওরা, ততক্ষণে সূর্য অস্ত গেছে। প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে চারদিক। ফকির একটা পিঠব্যাগ তুলে নিল, অন্যটা পিয়া নিজের কাঁধে ঝুলিয়ে নিল, তারপর টুটুলকে সামনে রেখে লাইন করে এগোতে লাগল আস্তে আস্তে। পিয়া শুধু ওদের দুজনের দিকে চোখ রেখে হেঁটে যাচ্ছিল, ফলে আশেপাশের দিকে খুব একটা নজর দিতে পারছিল না। চলতে চলতে হঠাৎ এক সময় থেমে গেল ফকির। বলল, “মাসিমা।” পিয়া তাকিয়ে দেখল একটা সিঁড়ির দিকে ইশারা করছে ও। একটা বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে শেষ হয়েছে সিঁড়িটা।
এই সেই জায়গা? ফকির কাঁধ থেকে ব্যাগটা নামিয়ে পিয়ার হাতে তুলে দিল। কী করা উচিত এখন? ওরা দুজনে একটু পিছিয়ে গেল। ফকিরের হাতে জালের মধ্যে কঁকড়ার পুঁটলি, আর কাপড়জামাগুলো বান্ডিল বেঁধে মাথায় তুলে নিয়েছে টুটুল। আবার হাত তুলে বন্ধ দরজাটার দিকে ইশারা করল ফকির। ওদের দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে বুঝতে পারল পিয়া, ওকে ওখানেই রেখে এখন ফিরে চলে যাবে ওরা। হঠাৎ কেমন যেন ভয় ভয় লাগল ওর। চেঁচিয়ে বলল, “ওয়েট। হোয়্যার আর ইউ গোয়িং?”
নানা রকম অদ্ভুত সব সম্ভাবনার কথা আগে থেকেই ঘুরপাক খাচ্ছিল পিয়ার মাথার ভেতরে, কিন্তু এরকম ভাবে ওকে একা দাঁড় করিয়ে রেখে একটা কথাও না বলে ওরা চলে যাবে, সেরকম যে কিছু হতে পারে তা কখনও ভাবেনি। এও মনে হয়নি যে ওদের চলে যাওয়ার সম্ভাবনার কথা ভাবতেই এরকম একটা শীতল একাকিত্বের অনুভূতি এসে পেয়ে। বসবে ওকে।
“ওয়েট। জাস্ট আ মিনিট।”
দূরে কোথাও একটা জেনারেটর চালু হল, আর পাশের একটা জানালা দিয়ে ঝকঝকে আলো এসে পড়ল ভেতর থেকে। এই ক’দিনে প্রাকৃতিক আলো-অন্ধকারেই সয়ে গিয়েছিল চোখ, হঠাৎ এই ফ্যাটফ্যাটে উজ্জ্বল ইলেকট্রিকের আলোয় মুহূর্তের জন্য যেন ধাঁধা লেগে গেল পিয়ার। দুয়েকবার পিটপিট করে দু’হাতের মুঠি দিয়ে চোখ কচলে নিল। নজর ফিরে পেতে তাকিয়ে দেখল চলে গেছে ওরা। দু’জনেই। ফকির আর টুটুল।
মনে পড়ল এখানে নিয়ে আসার জন্য ফকিরকে কোনও পারিশ্রমিক দেওয়া হয়নি। কী করে আবার খুঁজে পাওয়া যাবে ওকে? কোথায় থাকে ফকির সে তো জানে না পিয়া। ওর পুরো নামটা পর্যন্ত জিজ্ঞেস করে রাখা হয়নি। মুখের সামনে দু’হাত নিয়ে অন্ধকারের দিকে ফিরে চিৎকার করে একবার ডাকল, “ফকির!”
“কে?” জবাবটা এল একজন মহিলার গলায়, সামনে থেকে নয়, পেছন দিক থেকে। হঠাৎ খুলে গেল বন্ধ দরজাটা। পিয়া দেখল ছোট্টখাট্ট চেহারার বয়স্কা একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন ওর সামনে। মাথার চুলগুলো খড়ের আঁটির মতো, চোখে সোনালি ফ্রেমের একটা চশমা। “কে?”
দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল পিয়া। “কিছু মনে করবেন না, ঠিক জায়গাতে এসেছি কিনা জানি না, আসলে আমি মাসিমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছি।” মহিলা বুঝবেন কি বুঝবেন না সেসব না ভেবেই এক নিশ্বাসে হড়বড় করে ইংরেজিতে কথাগুলো বলে গেল পিয়া।
একটা অস্বস্তিকর মুহূর্ত। পিয়া টের পাচ্ছিল একজোড়া তীক্ষ্ণ সন্ধানী চোখ খুব ভাল করে জরিপ করে নিচ্ছে ওকে। নজর করল ওর নুনের দাগ-লাগা মুখ আর কাদামাখা সুতির প্যান্ট দেখতে দেখতে সোনালি ফ্রেম একবার ওপরে উঠছে, ফের নীচে নামছে। তারপর ওকে আশ্বস্ত করে বাঁশির মতো মিষ্টি সুরেলা ইংরেজিতে মহিলা বললেন, “একদম ঠিক জায়গাতেই এসেছ। কিন্তু তুমি কে বলো তো? আমি কি তোমাকে চিনি?”
“না,” পিয়া বলল, “আপনি আমাকে চিনবেন না। আমার নাম পিয়ালি রয়। আপনার ভাগ্নের সঙ্গে ট্রেনে আমার আলাপ হয়েছিল।”
“কানাই?”
“হ্যাঁ। উনিই আমাকে এখানে আসতে বলেছিলেন।”
“বেশ বেশ। ভেতরে এসো। কানাই এক্ষুনি নীচে নেমে আসবে।” একপাশে সরে গিয়ে পিয়াকে ভেতরে ঢোকার জায়গা করে দিলেন মহিলা। “কিন্তু তুমি চিনে চিনে এখানে এলে কী করে বলো তো? একা তো নিশ্চয়ই আসনি?”
“না, না। একা আমি জীবনে খুঁজে বের করতে পারতাম না।”
“তা হলে কার সঙ্গে এলে? বাইরে তো কাউকে দেখলাম না।”
“আপনি দরজা খুলতে খুলতেই চলে গেল ওরা–” কথাটা শেষ করার আগেই দড়াম করে খুলে গেল দরজাটা। কানাই ভেতরে এল। বিস্ময়ে চোখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, “আরে, পিয়া না?”
“হ্যাঁ।”
“আসতে পারলেন তা হলে?”
“চলে এলাম।”
“গুড, কানাই একগাল হাসল। এত তাড়াতাড়ি পিয়ার সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যাবে ভাবেনি ও। মনে মনে একটু খুশি হল কানাই, শ্লাঘাও বোধ করল একটু। লক্ষণটা মনে হল ভালই। “বেশ একটা ইভেন্টফুল ট্রিপ হয়েছে মনে হচ্ছে?” ভাল করে একবার পিয়ার কাদামাখা জামাকাপড়গুলো দেখল কানাই। “তা, কী করে এলেন এখানে?”
“একটা দাঁড়-টানা নৌকোয়।”
“দাঁড়-টানা নৌকোয়?”
“হ্যাঁ। আসলে আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর একটা অ্যাক্সিডেন্টে পড়েছিলাম।” লঞ্চ থেকে জলে পড়ে যাওয়া পর্যন্ত কী কী ঘটেছিল সংক্ষেপে বলল পিয়া। “আর তারপর সেই জেলেটি আমার পেছন পেছন জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল না হলে কী যে হত কে জানে। একগাদা জল খেয়ে ফেলেছিলাম আমি, কিন্তু ও ঠিক টেনেটুনে আমাকে নৌকোয় তুলে ফেলল। আমার তখন মনে হল ওই গার্ডদের লঞ্চে আবার গিয়ে ওঠাটা ঠিক নিরাপদ হবে না। ভাবলাম একটা আন্দাজে ঢিল মেরে দেখি, জেলেটিকে একবার জিজ্ঞেস করি ও মাসিমাকে চেনে কিনা। দেখলাম চেনে। তো, তখন বললাম ও যদি আমাকে লুসিবাড়িতে পৌঁছে দেয় তা হলে কিছু টাকা দেব। অনেক আগেই আমরা পৌঁছে যেতাম এখানে, কিন্তু মাঝরাস্তায় আবার কয়েকটা ঘটনা ঘটল।”
“কী ঘটল আবার?”
“প্রথমে তো দেখা হল এক দল ডলফিনের সঙ্গে। তারপর, আজ সকালে একটা কুমিরের খপ্পরে পড়েছিলাম।”
“আরে সর্বনাশ!” নীলিমা বলল, “কারও কিছু হয়নি তো??
“না। কিন্তু হতেই পারত। একটা দাঁড় দিয়ে তারপর ওটাকে মেরে তাড়াল জেলেটি। একেবারে অবিশ্বাস্য ব্যাপার,” বলল পিয়া।
“কী ভয়ংকর! কে ছিল জেলেটি? নাম বলেছে তোমাকে?” নীলিমা জিজ্ঞেস করল।
“হ্যাঁ, বলেছে। ওর নাম ফকির।”
“ফকির?” নীলিমা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। “ফকির মণ্ডল ছিল কি?”
“পদবি তো বলেনি।”
“একটা ছোট ছেলে ছিল কি সঙ্গে?”
“হ্যাঁ, ছিল,” পিয়া বলল। “টুটুল।”
“ও-ই,” কানাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল নীলিমা, “এতক্ষণে বোঝা গেল কোথায় ছিল ও।”
“ওর খোঁজ করা হচ্ছিল নাকি?”
“হ্যাঁ, কানাই বলল, “ফকিরের বউ ময়না এখানকার হাসপাতালে কাজ করে। সে বেচারির তত চিন্তায় চিন্তায় প্রায় পাগল হবার দশা।” :
“তাই নাকি? ছি ছি, মনে হয় আমারই জন্য এতটা দেরি হয়েছে। আমিই ওদের আটকে রেখেছিলাম এতক্ষণ, তা না হলে হয়তো আরও অনেক আগেই ফিরে আসত,” বলল পিয়া।
“যাক গে,” নীলিমা বলল ঠোঁট চেপে, “ভালয় ভালয় ফিরে যখন এসেছে আর চিন্তার কোনও কারণ নেই।”
“আশা করি নেই,” পিয়া বলল। “আমার জন্য ওকে কোনও রকম ঝামেলায় পড়তে হলে খুব খারাপ লাগবে আমার। দু-দু’বার ও আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। আর ও-ই তো সোজা ওই ডলফিনের ঝকটার কাছে নিয়ে গেল আমাকে।”
“তাই নাকি? কিন্তু আপনি যে ডলফিনের খোঁজ করছেন সেটা ও বুঝল কী করে?” জিজ্ঞেস করল কানাই।
“আমি ওকে ছবি দেখালাম, একটা ফ্ল্যাশকার্ড,” বলল পিয়া। “আর কিচ্ছু বলতে হয়নি ওকে। ও সোজা আমাকে ডলফিনগুলোর কাছে নিয়ে গেল। এক হিসেবে দেখতে গেলে ওই লঞ্চ থেকে পড়ে যাওয়াটা ভালই হয়েছিল আমার পক্ষে একা একা কিছুতেই আমি ওই ডলফিনগুলোকে খুঁজে পেতাম না। একবার দেখা করতেই হবে ওর সঙ্গে। অন্তত পয়সাটা তো ওকে দিতে হবে।”
“সে নিয়ে চিন্তা কোরো না,” নীলিমা বলল। “ওরা এই কাছেই থাকে, এই ট্রাস্টের কোয়ার্টারে। সকালে কানাই নিয়ে যাবে তোমাকে।”
কানাইয়ের দিকে মুখ ফেরাল পিয়া। “খুব ভাল হয় যদি পারেন।”
“হ্যাঁ হ্যাঁ, কেন পারব না?” বলল কানাই। “কিন্তু সে তো কাল সকালে। এখন আপাতত আপনার থাকা-টাকার একটা ব্যবস্থা করা যাক। জামাকাপড় পালটে রেস্ট নিন আপনি।”
এর পরে কী হবে তাই নিয়ে এতক্ষণ মাথাই ঘামায়নি পিয়া। এবার এখানে এসে পৌঁছনোর প্রাথমিক উত্তেজনাটুকু থিতিয়ে যেতে হঠাৎ এই ক’দিনের ক্লান্তির সমস্ত ভার যেন চেপে বসল ওর ওপর। “থাকার ব্যবস্থা?” ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল পিয়া। “কোথায়?”
“এখানেই। মানে, দোতলায়,” বলল কানাই।
একটু অস্বস্তি লাগছিল পিয়ার। কানাই কি মনে করেছে পিয়া এখানে কানাইয়ের সঙ্গে থাকবে?
“কাছাকাছি কোনও হোটেল-টোটেল নেই?”
“হোটেল এখানে নেই,” নীলিমা বলল। “তবে ওপরে একটা গেস্ট হাউস আছে, সেখানে তিনটে খালি ঘর আছে। তুমি স্বচ্ছন্দে থাকতে পার। আর কেউ নেইও ওপরে, কানাই ছাড়া। ও যদি তোমায় বিরক্ত করে, তুমি সোজা নীচে নেমে এসে আমাকে একবার খালি খবরটা দেবে।”
হেসে ফেলল পিয়া। “না না, সে ঠিক আছে। আর নিজের দেখভাল করার উপায় আমার জানা আছে। তবে মাসিমার কাছ থেকে আমন্ত্রণটা আসায় একটু খুশি হল পিয়া: রাজি হওয়াটা যেন সহজ হয়ে গেল এর ফলে। বলল, “থ্যাঙ্ক ইউ। সত্যি, একটা রাত একটু ভাল করে বিশ্রাম নেওয়া দরকার। আমি দিন কয়েক এখানে থাকলে সত্যি কোনও অসুবিধা হবে না তো আপনাদের?”
“তোমার যত দিন ইচ্ছে থাকো,” বলল নীলিমা। “কানাই তোমাকে ঘুরে ঘুরে সব দেখিয়ে দেবে।”
“চলে আসুন,” একটা পিঠব্যাগ হাতে তুলে নিয়ে বলল কানাই। “এই দিকে।” সিঁড়ি দিয়ে কানাই দোতলায় নিয়ে গেল ওকে। রান্নাঘর আর বাথরুমটা দেখিয়ে দিয়ে তালা খুলে দিল একটা ঘরের। সুইচ টিপে টিউব লাইটটা জ্বালিয়ে কানাই দেখল ওর নিজের শোয়ার ঘরটার সঙ্গে এটার তফাত কিছু নেই। এখানেও সেই দুটো সরু সরু তক্তপোশ, প্রত্যেকটার সঙ্গে একটা করে মশারি লাগানো। দেয়ালে কোথাও কোথাও নতুন প্লাস্টার, অনেক জায়গায় গত বর্ষার সময়কার ড্যাম্পের ছোপ, ফাটল ধরেছে কিছু কিছু জায়গায়। উলটোদিকে গরাদ দেওয়া একটা জানালা। ট্রাস্টের কম্পাউন্ডের লাগোয়া ধানজমিগুলি দেখা যাচ্ছে জানালা দিয়ে।
“চলবে এতে?” একটা তক্তপোশের ওপরে পিয়ার পিঠব্যাগটা রেখে জিজ্ঞেস করল কানাই।
ঘরের ভেতরে ঢুকে চারদিকটা একবার দেখল পিয়া। এমনিতে যদিও খালি খালি, কিন্তু যথেষ্টই আরামদায়ক ঘরখানা : চাদরগুলি পরিষ্কার, এমনকী বিছানার পায়ের কাছে একটা কাঁচা তোয়ালেও ভাঁজ করে রাখা আছে। জানালার পাশে একটা টেবিল আর খাড়া-পিঠ চেয়ার। দরজাটা শক্তপোক্ত দেখে খুশি হল পিয়া। ভেতর থেকে ছিটকিনি লাগানোর ব্যবস্থাও আছে।
“এত কিছু সত্যি আমি আশা করিনি,” পিয়া বলল। “অনেক ধন্যবাদ।”
মাথা নাড়ল কানাই, “ধন্যবাদ জানানোর কোনও প্রয়োজন নেই। আপনি আসাতে ভালই হয়েছে। একা একা একটু একঘেয়ে লাগছিল আমার।”
কী জবাব দেওয়া উচিত এ কথার বুঝতে না পেরে নিরপেক্ষ একটা হাসি হাসল পিয়া। “ঠিক আছে, নিজের মতো করে দেখেশুনে নিন,” বলল কানাই, “আমি ওপরের তলায় আছি, আমার মেসোর পড়ার ঘরে। কিছু দরকার লাগলে বলবেন।”
.
ভোজ
যে-কোনও একটা ছুতো পেলেই আবার মরিচঝাঁপি যাওয়ার জন্য মনে মনে তৈরিই। ছিলাম আমি, কিন্তু হরেন যে সুযোগ করে দিল তার চেয়ে ভাল অজুহাত আর কিছু হতে পারত না। ইতোমধ্যে ওর ছেলের ভর্তির ব্যবস্থাও করে দিয়েছি, ফলে স্কুলের আশেপাশে প্রায়ই দেখা হয়ে যেত আমার ওর সঙ্গে।
একদিন হরেন বলল, “সার, মরিচঝাঁপি থেকে খবর আছে। ওরা একদিন একটা ফিস্টির ব্যবস্থা করেছে ওখানে, কুসুম বার বার করে আপনাকে যেতে বলে দিয়েছে।”
আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমি। “ফিস্টি? কীসের ফিস্টি?”
“কলকাতা থেকে অনেক সব লোককে ওরা নেমন্তন্ন করেছে–কবি, লেখক, খবরের কাগজের লোকজন সব আসবে। ওদেরকে ওরা দ্বীপটার কথা বলবে, কী কী করেছে ওখানে সব দেখাবে।”
এতক্ষণে পরিষ্কার হল পুরো ব্যাপারটা : ওই উদ্বাস্তু নেতাদের বিচারবুদ্ধি দেখে নতুন করে আবার মুগ্ধ হলাম আমি। দেখা যাচ্ছে, ওরা বুঝতে পেরেছে যে এখানে টিকে থাকতে গেলে নিজেদের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে হবে। আর এ হল তারই প্রথম পদক্ষেপ। যেতে তো আমাকে হবেই। হরেন বলল ভোর থাকতেই বেরিয়ে পড়তে হবে। বললাম, আমি তৈরি হয়ে থাকব।
বাড়ি ফিরলাম যখন, নীলিমা এক পলক আমার মুখের দিকে তাকিয়েই বলল, “কী ব্যাপার? এরকম দেখাচ্ছে কেন তোমাকে আজকে?”
কেন এর আগে মরিচঝাঁপি নিয়ে নীলিমার সঙ্গে কোনও কথা বলিনি আমি? বোধ হয় মনে মনে আমি জানতাম নীলিমা কিছুতেই আমার এই উৎসাহের শরিক হবে না; হয়তো আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে ওদের নিয়ে আমার এই উত্তেজনাকে লুসিবাড়িতে ওর এতদিনের কাজের প্রতি এক ধরনের বিশ্বাসভঙ্গ বলে মনে করবে। যাই হোক না কেন, আমার এই ভয় অচিরেই সত্যি বলে প্রমাণিত হল। এই উদ্বাস্তুদের মরিচঝাঁপিতে এসে ওঠার ঘটনাটার মধ্যে যে নাটকীয়তা আছে, আমার পক্ষে যতটা সম্ভব তা বর্ণনা করলাম; কীসের টানে মধ্য ভারতের নির্বাসন থেকে এই ভাটির দেশে এসে উপস্থিত হয়েছে ওরা সেটা ব্যাখ্যা করলাম; ওদের সব পরিকল্পনা, নতুন ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন, নতুন বাসভূমি গড়ে তোলার জন্য অটল সংকল্প–সব বুঝিয়ে বললাম ওকে।
আমাকে অবাক করে দিয়ে নীলিমা বলল মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুদের আসার কথা ও জানে : এ খবর ও পেয়েছে কলকাতায়, বিভিন্ন আমলা আর নেতাদের কাছ থেকে। ও বলল সরকারি লোকেদের চোখে ওই উদ্বাস্তুরা স্রেফ বেআইনি দখলদার; ওদের ওখানে থাকতে দেবে না সরকার; গণ্ডগোল একটা হবেই।
আমাকে বলল, “নির্মল, আমি চাই না যে তুমি ওখানে যাও। ওই রিফিউজিদের সঙ্গে আমার কোনও বিরোধ নেই, কিন্তু তুমি এসব ঝুটঝামেলার মধ্যে যাও সেটা আমি চাই না।”
সেই মুহূর্তেই খুব দুঃখের সঙ্গে আমি বুঝতে পারলাম, এখন থেকে আমাকে গোপনেই যোগাযোগ রাখতে হবে মরিচঝাঁপির সঙ্গে। আমার ইচ্ছে ছিল পরের দিনের ফিস্টের কথাটা ওকে বলব, কিন্তু এরপর সে কথা আর তুললাম না। নীলিমাকে যদ্র চিনি, ও ঠিক কোনও না কোনও উপায়ে আমার যাওয়াটা আটকে দেবে।
তা সত্ত্বেও ও চাপাচাপি না করলে মিথ্যে বলার কোনও বাসনা আমার ছিল না। আমাকে ঝোলা গোছাতে দেখে জিজ্ঞেস করল আমি কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা করছি কিনা।
“হ্যাঁ, কাল সকালেই বেরোতে হবে আমাকে।” বানিয়ে বানিয়ে বললাম মোল্লাখালিতে একটা স্কুলে নিমন্ত্রণ আছে।
স্পষ্ট বুঝতে পারলাম আমার কথা বিশ্বাস করল না নীলিমা। খুব ভাল করে আমাকে একবার দেখে নিয়ে বলল, “তাই? তো, কার সঙ্গে যাবে শুনি?”
“হরেনের সঙ্গে,” বললাম আমি।
“তাই নাকি? হরেনের সঙ্গে?” ওর গলার বাঁকা সুরটা শুনেই ভয় হল আমার । মনে হল শেষ পর্যন্ত বোধহয় ফাস হয়ে যাবে আমার গোপন কথাটা।
এই ভাবেই আমাদের দু’জনের সম্পর্কের মধ্যে অবিশ্বাসের জন্ম হল সেদিন।
কিন্তু ফিস্টটাতে আমি গেলাম। আমার সারা জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় দিনগুলির অন্যতম হয়ে থাকবে সেই দিনটা। আমি যদি কলকাতাতেই থেকে যেতাম তা হলে আমার জীবন কী রকম হত সেটা যেন সেদিন, অবসরের ঠিক আগের মুহূর্তে, এক ঝলক দেখতে পেলাম আমি। শহর থেকে অতিথি যারা এসেছিলেন সে রকম সব মানুষদের সঙ্গেই তো ওঠাবসা হত আমার : সাংবাদিক, আলোকচিত্রী, বিখ্যাত লেখক; তাদের মধ্যে ছিলেন সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সাংবাদিক জ্যোতির্ময় দত্ত। এমনকী আমার চেনাশোনা লোকও ছিল কয়েকজন, ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় যোগাযোগ ছিল ওদের সঙ্গে। একজন ছিল আমার এক সময়কার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং কমরেড–আমরা তখন খোকন বলে ডাকতাম তাকে। দূর থেকে ওকে সেদিন দেখলাম আমি। কী সুন্দর চেহারা হয়েছে ওর : কুচকুচে কালো চুল, মুখ থেকে যেন জ্যোতি ফুটে বেরোচ্ছে। যদি সাহিত্যচর্চা ছেড়ে না দিতাম, আমিও কি তা হলে আজকে এরকম জায়গায় পৌঁছতাম?
সারা জীবনের না করা কাজগুলোর জন্য সেদিন যেমন অনুতাপ হল সেরকম আমার আগে আর কখনও হয়নি।
উদ্বাস্তু নেতারা যখন অতিথিদের নিয়ে দ্বীপটা ঘুরে দেখাতে বেরোল, একটু দূর থেকে আমিও চললাম ওদের পেছন পেছন। কত কিছু যে দেখানোর আছে এমনকী আমি আগেরবার যখন এসেছিলাম তারপর থেকে এই ক’দিনে আরও কত কী করেছে ওরা। অনেক কাজ করে ফেলেছে এর মধ্যে। নুনের ভাটি তৈরি হয়েছে, টিউবওয়েল বসানো হয়েছে, আল দিয়ে জল আটকে মাছ চাষের ব্যবস্থা হয়েছে, একটা রুটি কারখানা চালু হয়েছে, নৌকোর মিস্ত্রিদের কাজের জায়গা তৈরি হয়েছে, মাটির জিনিস গড়ার জায়গা করা হয়েছে, কামারশালা খুলেছে, আরও কত কী। কিছু লোক নৌকো তৈরি করছে, কয়েকজন বসে জাল বুনছে, কাঁকড়া ধরার দোন বানাচ্ছে; ছোট ছোট বাজার মতো বসেছে কয়েকটা জায়গায়, সেখানে জিনিসপত্র কেনাবেচা হচ্ছে। এই সব কিছু হয়েছে মাত্র এই কয়েক মাসে! এ এক আশ্চর্য দৃশ্য–যেন এই কাদামাটির ওপর হঠাৎ করে একটা নতুন সভ্যতা গজিয়ে উঠেছে।
তারপরে ফিস্ট। সাবেকি ধরনে সুন্দর করে গুছিয়ে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, মাটিতে কলাপাতা পেতে গাছের ছায়ায় আসন দেওয়া হয়েছে অতিথিদের। যারা পরিবেশন করছিল তাদের মধ্যে কুসুমকে দেখতে পেলাম আমি। ও আমাকে। দেখাল কী বিশাল বিশাল সব ডেকচি আনা হয়েছে রান্নার জন্য। কত রকমের যে মাছ রাঁধা হয়েছে বড় বড় চিংড়ি, গলদা বাগদা দু’রকমেরই, তা ছাড়াও ট্যাংরা, ইলিশ, পার্শে, পুঁটি, ভেটকি, রুই আর চিতল।
একেবারে হতবাক হয়ে গেলাম আমি। অধিকাংশ লোকেরই এখানে দু’বেলা ভাত জোটে না, সে তো আমি ভাল করেই জানি। বুঝতে পারলাম না কী করে এই বিশাল ব্যবস্থা করল এরা।
কোথা থেকে এল এত সব? জিজ্ঞেস করলাম কুসুমকে।
যে যতটুকু পেরেছে দিয়েছে, ও বলল। বিশেষ কিছু তো কিনতে হয়নি–শুধু চালটা। বাকি সব তো নদী থেকেই এসেছে। কালকে পর্যন্ত আমরা সবাই জাল নিয়ে, ছিপ নিয়ে মাছ ধরেছি। বাচ্চারাও পর্যন্ত। পার্শে মাছগুলো দেখিয়ে খানিকটা গর্বের সঙ্গে বলল, “আজকে সকালে ছ’টা এই মাছ ধরেছে ফকির।”
আমি বিস্ময়বিমুগ্ধ। শহুরে মানুষদের হৃদয় জয় করার জন্য টাটকা মাছের চেয়ে ভাল আর কি হতে পারে? অতিথিদের ঠিক বুঝেছে তো এরা!
কুসুম আমাকে বার বার বলল বসে পড়তে, কিন্তু আমি ঠিক পারলাম না। এই অতিথিদের সঙ্গে এক পঙক্তিতে আমি কী করে বসব? “না রে কুসুম,” বললাম। আমি। “যাদের খাইয়ে কাজ হবে তাদের খাওয়া। এত দামি খাবার আমাকে খাইয়ে কেন নষ্ট করবি খামখা?” একটা গাছের ছায়ায় বসে বসে দেখতে লাগলাম আমি। মাঝে মাঝে কুসুম কি ফকির এসে কলাপাতায় মুড়ে অল্প কিছু কিছু খাবার দিয়ে যেতে লাগল আমাকে।
একটু পরেই বোঝা গেল যে ওষুধে কাজ দিয়েছে : অতিথিরা একেবারে মুগ্ধ। উদ্বাস্তুদের কাজকর্মের গুণগান করে অনেক সব বক্তৃতা দেওয়া হল। সবাই এক বাক্যে স্বীকার করল যে মরিচঝাঁপিতে যা ঘটছে তার গুরুত্ব শুধু এই দ্বীপটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আজকে মরিচঝাঁপিতে যে বীজ বোনা হয়েছে, কে বলতে পারে তার থেকেই একদিন দলিতদের জন্য নতুন রাষ্ট্র না হলেও, অন্তত দেশের সমস্ত নিপীড়িত মানুষের জন্য নিশ্চিন্ত কোনও এক আশ্রয়স্থল গড়ে উঠবে না?
বেলা যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তখন আস্তে আস্তে খোকনের কাছে গিয়ে ওর চোখের সামনে দাঁড়ালাম আমি। ও এক পলক দেখল আমাকে, কিন্তু চিনতে পারল না। অন্যদের সঙ্গে যেমন কথা বলছিল, বলতেই থাকল। খানিক পরে গিয়ে ওর কনুইয়ে আলতো করে টোকা দিলাম একটা। বললাম, “এই যে, খোকন!”
অচেনা একজন লোকের কাছ থেকে এরকম অতি পরিচিতের মতো সম্বোধন শুনে ও বিরক্ত হল একটু। বলল, “কে মশাই আপনি?”
যখন বললাম আমি কে, ওর মুখটা হাঁ হয়ে ঝুলে গেল, আর সেই হা-এর ভেতরে জিভটা জালে পড়া মাছের মতো লটপট করতে লাগল। “তুই?” অবশেষে বাক্স্ফুর্তি হল ওর। “তুই?”
“হ্যাঁ, আমি।”
“এত বছর কোনও খবর নেই তোর, আমরা তো সবাই ভেবেছিলাম–”
“কী? মরে গেছি? দেখতেই পাচ্ছিস দিব্যি জলজ্যান্ত দাঁড়িয়ে আছি তোর সামনে।”
মনে হল ও প্রায় বলে ফেলতে যাচ্ছিল, “মরলেই ভাল হত,” কিন্তু বলল না শেষ পর্যন্ত।
“কিন্তু এত বছর ধরে কী করছিলি তুই? কোথায় ছিলি?”
মনে হল আমার গোটা অস্তিত্বটার জন্যই যেন কৈফিয়ত চাওয়া হচ্ছে, যেন লুসিবাড়িতে এতগুলো বছর কী করে কাটিয়েছি তার হিসেব দিতে বলা হচ্ছে আমাকে।
কিন্তু ভদ্রতা রেখেই জবাবটা দিতে হল : “ইস্কুল মাস্টারি করছিলাম। এই কাছেই একটা জায়গায়।”
“আর লেখালিখি?”
কাঁধ ঝাঁকালাম আমি। কী আর বলব? “ভালই করেছি ছেড়ে দিয়ে,” বললাম অবশেষে।
“তোরা যা লিখছিস তার কাছে দাঁড়াতে পারত না আমার ওই সব লেখা।”
হায় লেখককুল! সামান্য তোষামোদেই কেমন গলে জল হয়ে যায়। আমার কাঁধে হাত দিয়ে ওখান থেকে একটু সরে এল ও। তারপর খানিকটা প্রশ্রয় দেওয়ার ভঙ্গিতে গলাটা একটু নামিয়ে–যেন বড়ভাই কথা বলছে ছোটভাইয়ের সঙ্গে, সেইভাবে–জিজ্ঞেস করল, “আচ্ছা নির্মল, এইসব রিফিউজিদের সঙ্গে তোর কী করে যোগাযোগ হল?”
বললাম, “আসলে এদের দু’-এক জনকে আমি চিনি। আর, রিটায়ার করারও সময় এসে গেছে, ভাবছিলাম এইখানে এসে এবার একটু আধটু মাস্টারি করব।”
“এইখানে?” খোকনের গলায় একটু দ্বিধার সুর। “কিন্তু সমস্যা হল, ওদের তো বোধহয় থাকতে দেওয়া হবে না এ জায়গায়।”
“ওরা তো আছেই এখানে,” আমি বললাম। “এখন কি আর সরানো সম্ভব নাকি ওদের? রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে তো তা হলে।”
হাসল খোকন। “ভুলে গেছ বন্ধু, সে সময়ে কী বলতাম আমরা?”
“কী বলতাম?”
“ডিম না ভেঙে ওমলেট বানানো যায় না।”
বাঁকা হাসি হাসল খোকন। এরকম হাসি একমাত্র তারাই হাসতে পারে যারা এক সময়ে আদর্শের কথা বলেছে কিন্তু কখনও সেই আদর্শে বিশ্বাস করেনি, আর ভেবেছে অন্য সকলেও তাদেরই মতো বিশ্বাসহীন আদর্শের কথা প্রচার করে চলেছে। একবার ভাবলাম যা তা বলে দিই মুখের ওপর, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই কেউ যেন প্রচণ্ড একটা ধাক্কা দিয়ে আমাকে মনে করিয়ে দিল যে অতখানি গর্বিত হওয়ার অধিকার আমার নেই। নীলিমা যেমন বিশাল কাজ করেছে এই কয় বছরে। কিন্তু আমি কী করেছি? সারা জীবনে কী কাজটা করেছি আমি? উত্তর খোঁজার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুই মনে এল না।
বিকেল হয়ে গেছে। হরেন আর কুসুম বেরিয়েছে দেখতে যদি কিছু মাছ পাওয়া যায়। ফকির বসে আছে একটা কাঁকড়া ধরার সুতো নিয়ে। ভাটির দেশে এই সুতোগুলোকে বলে দোন। সুতোটা নিয়ে ওর খেলা করা দেখতে দেখতে আমার বুকের ভেতরটা যেন উথলে উঠল। কত কী বলার আছে, কত কথা ঘুরপাক খাচ্ছে আমার মাথার মধ্যে, সেগুলি কি সব না বলাই রয়ে যাবে? ওঃ, কতগুলো বছর অকারণে নষ্ট হয়েছে, জীবনের কতটা সময় অকারণে জলাঞ্জলি দিয়েছি। রিলকের কথা মনে পড়ল আমার, বছরের পর বছর কেটে গেছে একটা শব্দও লিখতে পারেননি, তারপর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সমুদ্রের তীরে এক দুর্গে বসে লিখে ফেললেন দুইনো এলিজির কতগুলো কবিতা। নিস্তব্ধতাও আসলে প্রস্তুতির একটা অঙ্গ। একেকটা মিনিট কাটছে, আর আমার মনে হচ্ছে ভাটির দেশের প্রতিটি খুঁটিনাটি যেন চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বলতায় স্পষ্ট হয়ে উঠছে আমার সামনে। মনে হল ফকিরকে বলি, “জানিস কি তুই, প্রতিটা দোনে হাজারটা করে টোপ থাকে? তিন হাত ছাড়া ছাড়া বাঁধা হয় একেকটা টোপ? প্রত্যেকটা দোন তাই তিন হাজার হাত লম্বা?”
কবি যে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন তা ছাড়া আর কীভাবে এই জগৎটার যশোকীর্তন করি বলো? সেই পথে চলতে গেলে আমাদের কুমোর আর মজুরের কথা বলতে হবে, বলতে হবে
‘বরং এমন-কিছু তুলে ধরো,
যা সহজ, আর বংশপরম্পর স্বচ্ছন্দে নূতন রূপ নিতে-নিতে
এখন যা আমাদেরই অংশ হয়ে আমাদের হাতে, চোখে প্রাণবন্ত।’
.
আলাপ
স্নান সেরে জানালার পাশে চেয়ারটায় গা ডুবিয়ে বসল পিয়া। খানিক পরে দেখল ওর আর ওঠার ক্ষমতা নেই। এই কদিন স্রেফ উবু হয়ে আর আসন করে বসে থাকার পর একটা হেলান দেওয়ার জায়গা পেয়ে কেমন যেন এক অদ্ভুত আরামের অনুভূতি হচ্ছে। ইচ্ছেমতো পা-ও দোলানো যাচ্ছে–পড়ে যাওয়ার কোনও ভয় নেই। এখনও মনে হচ্ছে নৌকোর দুলুনি টের পাচ্ছে সারা শরীরে, কানে বাজছে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাসের ঝিরঝির শব্দ।
নৌকোয় চলার বোধটা ফেরত আসতেই হঠাৎ সকালের সেই ভয়ংকর ঘটনার কথা মনে পড়ে গা শিউরে উঠল পিয়ার। মাত্রই কয়েকঘন্টা আগের ঘটনা অনুভূতিগুলি যেন এখনও স্মৃতি হয়ে যায়নি; টাটকা, স্পষ্ট রয়ে গেছে মনের মধ্যে। পরিষ্কার দেখতে পেল পিয়া কুমিরটার মাথা মোচড় খেয়ে ঘুরে যাচ্ছে শূন্যে, দেখতে পেল এক মুহূর্ত আগেও ওর কবজিটা যেখানে ছিল ঠিক সেইখানটায় এসে খপাত করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সরীসৃপটার হাঁ মুখ : হাতটা ধরে ফেলবে বলে এত নিশ্চিত ছিল কুমিরটা, যে ওকে ডিঙি থেকে টেনে জলের ভেতরে নিয়ে যাওয়ার জন্য শরীরের চলন যেরকম হওয়া দরকার ঠিক সেইভাবেই লাফ দিয়েছিল ওটা। পিয়া কল্পনা করল একটানে ওকে জন্তুটা নিয়ে চলে যাচ্ছে জলের নীচে, একবার মুহূর্তের জন্য আলগা হচ্ছে কামড়, তারপর ওর শরীরের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় এসে ফের বন্ধ হচ্ছে হাঁ-মুখ। দ্রুত ওকে নিয়ে চলে যাচ্ছে সেই অদ্ভুত উজ্জ্বল গভীরে, যেখানে সূর্যের আলোর কোনও দিক-দিশা নেই, যেখানে বোঝা যায় না কোনদিকে গেলে ওপরে ওঠা যাবে, আর কোনদিকে গেলে তলিয়ে যাবে আরও নীচে। লঞ্চ থেকে পড়ে যাওয়ার সময়কার আতঙ্কের কথা মনে পড়ে গেল ওর, মনে পড়ল সেই শরীর অবশ করা ভয়ের কথা, যখন চেতনার মধ্যে একটাই কথা বাজতে থাকে–এই অতল কারা থেকে মুক্তির কোনও উপায় নেই। পর পর এই সব দৃশ্যগুলো চোখের সামনে এসে এমন এক স্পষ্ট জীবন্ত মন্তাজ তৈরি হল যে পিয়ার হাত আবার থরথর করে কাঁপতে শুরু করল। আর ফকিরের অনুপস্থিতিতে ঘটনাগুলিকে তখনকার থেকে অনেক বেশি ভয়াবহ মনে হল এখন।
জোর করে উঠে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল পিয়া। এখনও চাঁদ ওঠেনি, অন্ধকারে ঝুপসি কয়েকটা নারকেলগাছ আবছা নজরে আসছে, তার পরেই ফসল কাটা ন্যাড়া জমির বিস্তীর্ণ শূন্যতা। বাড়ির সামনের দিক থেকে একটা কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে আসছে : কোনও মহিলার গলা আর তার সঙ্গে কানাইয়ের ভারী গম্ভীর কণ্ঠস্বর।
চেয়ার থেকে শরীরটাকে টেনে তুলে একতলায় নেমে এল পিয়া। দরজাটার সামনে হাতে একটা লণ্ঠন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কানাই লাল শাড়ি পরা এক মহিলার সঙ্গে কথা বলছে। খানিকটা অন্যদিকে ফিরে দাঁড়িয়েছিল মহিলা, পিয়াকে আসতে দেখে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে কানাইয়ের লণ্ঠনের আলোয় হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখের একটা পাশ। পিয়া দেখল ওরই কাছাকাছি বয়স হবে মেয়েটির, ভরা শরীর, চওড়া হাঁ মুখ আর বড় বড় ঝকঝকে দুটো চোখ। দুই ভুরুর মাঝে বড় একটা লাল টিপ আর মাথায় চকচকে কালো চুলের মাঝখান দিয়ে একটা ক্ষতচিহ্নের মতো মোটা করে টকটকে লাল সিঁদুরের দাগ।
“আরে এই যে পিয়া”, কানাই বলল ইংরেজিতে। ওর গলায় বাড়তি উচ্ছ্বাসের সুরটা থেকে পিয়া আন্দাজ করল ওকে নিয়েই কথা হচ্ছিল এতক্ষণ। দেখল মেয়েটি স্পষ্ট স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে, যেন বুঝতে পেরেছে ও কে, আর মনে মনে যাচাই করে নিচ্ছে ওকে। তারপর ওই খোলা নজরে জরিপ করার মতোই অস্বস্তিকর ভঙ্গিতে হঠাৎ অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল মুখটা। কানাইয়ের হাতে কয়েকটা স্টেনলেস স্টিলের কৌটো ধরিয়ে দিয়ে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে; তারপর অন্ধকারে ঢাকা ট্রাস্ট চৌহদ্দির মধ্যে মিলিয়ে গেল কোথায়।
“কে ওই মহিলা?” পিয়া জিজ্ঞেস করল কানাইকে।
“বলিনি আপনাকে? ও তো ময়না, ফকিরের বউ।”
“তাই বুঝি?”
ফকিরের বউয়ের চেহারা যেমন কল্পনা করেছিল পিয়া তার থেকে ময়না এতটাই আলাদা যে ব্যাপারটা হজম করতে একটু সময় লাগল ওর। তারপর বলল, “বোঝা উচিত ছিল আমার।”
“কী বোঝা উচিত ছিল?”
“যে ও ফকিরের বউ। ছেলেটার চোখদুটো ঠিক ওর মতো।”
“তাই নাকি?”
“হ্যাঁ,” বলল পিয়া। “কী বলতে এসেছিল ও?”।
“এই যে, এই টিফিন ক্যারিয়ারটা দিয়ে গেল,” স্টিলের কৌটোগুলো তুলে দেখাল কানাই। “আমাদের রাতের খাবার আছে এর মধ্যে। হাসপাতালের রান্নাঘর থেকে ময়না নিয়ে এসেছে আমাদের জন্য।”
মুহূর্তের জন্য কানাইয়ের ওপর থেকে মনোযোগ সরে গেল পিয়ার। ওই মেয়েটির কথা ভাবছিল ও, ফকিরের বউয়ের কথা। ফকির আর টুটুলের কাছে ফিরে গেল বউটি, আর ওকে ফিরে যেতে হবে গেস্ট হাউসের দোতলার শূন্যতায় ভেবে অল্প একটু ঈর্ষা হল মনে। এই চিন্তায় নিজেরই লজ্জা লাগল পিয়ার, আর সেটা ঢাকার জন্য ও কানাইয়ের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে তাড়াতাড়ি বলল, “আমি যেরকম ভেবেছিলাম তার সঙ্গে কোনওই মিল নেই ওর।”
“মিল নেই?”
“না।” আবার পিয়া দেখল ঠিক উপযুক্ত শব্দটা কিছুতেই মনে আসছে না। বলল, “মানে, বেশ ভালই দেখতে, না?”
“আপনার তাই মনে হল?”
বুঝতে পারছিল পিয়া এ প্রসঙ্গটা এখানেই শেষ করে দেওয়া ভাল, কিন্তু তাও থামল না, ক্ষতস্থানের ওপর থেকে মামড়ি খুঁটে তোলার মতো বলেই যেতে লাগল : “তাই তো। বেশ সুন্দরীই বলা চলে।”
“ঠিকই বলেছেন, নিজেকে সামলে নিয়ে একটু মোলায়েম সুরে বলল কানাই। “খুবই অ্যাট্রাক্টিভ। কিন্তু আরও গুণ আছে ওর সেসব দেখতে গেলে খুব একটা সাধারণ মেয়ে নয় ময়না।”
“তাই নাকি? কী রকম?”
“অদ্ভুত ওর জীবনের কাহিনি,” বলল কানাই। “অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে থেকেও নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখেছে, শিগগিরই হয়তো পুরোদস্তুর নার্স হয়ে যাবে এই হাসপাতালে, নিজের এবং পরিবারের জন্য ও ঠিক কী চায় সেটা ও জানে, এবং সেটা অর্জন করার জন্য যে-কোনও বাধাকে তুচ্ছ করে এগিয়ে যাওয়ার জোর ওর আছে। ওর মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে, এক ধরনের বলিষ্ঠতা আছে। অনেকদূর যাবে ওই মেয়ে।”
কানাইয়ের কথার মধ্যে কোথায় যেন একটা তুলনামূলক বিচারের আভাস রয়েছে মনে হল। সেই বিচারে ও নিজে কোন জায়গায় দাঁড়াবে মনে মনে না ভেবে পারল না পিয়া–ওর কখনওই বিশেষ কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না, আর পড়াশোনা শেখার জন্যও কখনও নিজের চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করতে হয়নি। ও জানে, কানাইয়ের চোখে ও একটা নরম-সরম, বাপ-মার আদরে মানুষ হওয়া সাদামাটা ধরনের মেয়ে। তবে এই ভাবে ওকে বিচার করার জন্য কানাইকে দোষ দেয় না পিয়া; কানাইয়ের সম্পর্কেও তো ওর যেমন মনে হয় যে বিশেষ একটা ধাঁচের ভারতীয় ছেলেরা যে রকম হয় সেই রকম ধরনের মানুষ ও–দাম্ভিক, আত্মকেন্দ্রিক, জোর করে নিজের মতামত অন্যের ওপর চাপিয়ে দিতে আগ্রহী–তবু, এ সব কিছু সত্ত্বেও অপছন্দ করার মতো নয়।
এবার একটা নিরাপদ দিকে কথা ঘোরাল পিয়া, “ওরা কি এই লুসিবাড়িরই লোক? ফকির আর ময়না?”
“না,” কানাই বলল। “ওদের দুজনেরই বাড়ি ছিল অন্য একটা দ্বীপে, সাতজেলিয়ায়। এখান থেকে অনেকটা দূরে।”
“তা হলে ওরা এখানে কেন থাকে?”
“একটা কারণ হল ময়না এখানে নার্সিং-এর ট্রেনিং নিচ্ছে, আর একটা কারণ হচ্ছে ও ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে চায়। ফকির টুটুলকে নিয়ে মাছ ধরতে চলে গিয়েছিল বলেই তাই রেগে গেছে ময়না।”
“দু’দিন ধরে আমিও যে ছিলাম ওই নৌকোতে সেটা ও জানে?”
“জানে,” বলল কানাই। “সবই জানে–ফরেস্ট গার্ড টাকা নিয়ে নিয়েছিল, আপনি জলে পড়ে গিয়েছিলেন, আপনাকে বাঁচাতে ফকির ঝাঁপ দিয়েছিল–সব। কুমিরের ঘটনাটাও জানে দেখলাম–বাচ্চাটা সব বলেছে ওকে।”
কানাই যে শুধু বাচ্চার কথাটাই উল্লেখ করছে সেটা লক্ষ করল পিয়া : তার মানে কি ফকির ময়নাকে বিশেষ কিছু বলেনি এই দু’দিনের ঘটনা সম্পর্কে, না কি ও অন্য রকম কিছু বিবরণ দিয়েছে? এই দুটো প্রশ্নের কোনওটারই উত্তর কানাইয়ের জানা আছে কিনা বুঝতে পারল না পিয়া, কিন্তু জিজ্ঞেসও করে উঠতে পারল না নিজে থেকে। তার বদলে বলল, “ময়না নিশ্চয়ই ভাবছে আমি কী করতে এসেছি এখানে?”
“সে তো বটেই,” বলল কানাই। “আমাকে জিজ্ঞেসও করল। আমি বললাম যে আপনি একজন বৈজ্ঞানিক। খুব ইমপ্রেসড হল ও।”
“কেন?”
“বুঝতেই পারছেন, লেখাপড়া সংক্রান্ত যে-কোনও বিষয়েই ওর খুব আগ্রহ।”
“ওকে বললেন নাকি যে আমরা কাল যাব ওদের বাড়িতে?”
“বললাম,” কানাই জবাব দিল। “ওরা থাকবে বাড়িতে, অপেক্ষা করবে আমাদের জন্য।” কথা বলতে বলতে দোতলায় গেস্ট হাউসে উঠে এসেছে কানাই আর পিয়া। হাতের টিফিন ক্যারিয়ারটা টেবিলের ওপর রাখল কানাই। “নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছে আপনার?” বাটিগুলো আলাদা করতে করতে জিজ্ঞেস করল ও। “সব সময় এত খাবার নিয়ে আসে ময়না–আমাদের দুজনের কুলিয়ে বেশি হয়ে যাবে। দেখি কী এনেছে–ভাত আছে, ডাল আছে, মাঝের ঝোল আছে, চচ্চড়ি আর বেগুন ভাজা। নিন, কী দিয়ে শুরু করবেন?”
পাত্রগুলোর দিকে একটু সংশয়ের দৃষ্টিতে তাকাল পিয়া। বলল, “কিছু মনে করবেন না আশা করি, কিন্তু এগুলোর একটাও কিছু খাওয়ার সাহস নেই আমার। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে আমাকে খুব সাবধানে থাকতে হয়।”
“এমনি ভাত খান হলে একটু,” কানাই বলল। “সেটা তো খেতেই পারেন?” মাথা নাড়ল পিয়া। “হ্যাঁ, সেটা হয়তো খেতে পারি একটু–শুধু প্লেন, সাদা ভাত।”
“এই নিন।” কয়েক হাতা ভাত পিয়ার প্লেটে তুলে দিল কানাই। একটা চামচও দিল। তারপর জামার হাতাটা গুটিয়ে, নিজের থালাতে খানিকটা ভাত নিয়ে খেতে শুরু করল হাত দিয়ে।
খেতে খেতে লুসিবাড়ির বিষয়ে অনেক কথা বলল কানাই। ড্যানিয়েল হ্যামিলটনের কথা বলল, কী করে এই দ্বীপে বসতি শুরু হল সে কথা বলল, নির্মল আর নীলিমা কীভাবে এখানে এসেছিল সেই গল্প করল। জায়গাটার বিষয়ে ও এত্ব কিছু জানে দেখে শেষে পিয়া জিজ্ঞেস করল, “আপনার কথা শুনতে শুনতে মনে হচ্ছে যেন আপনি বহু দিন কাটিয়েছেন এখানে। কিন্তু সেটা তো ঠিক নয়, তাই না?”
পিয়ার বক্তব্য সমর্থন করল কানাই, “একেবারেই না। আমি এর আগে একবার মাত্র এসেছিলাম এখানে। ছোটবেলায়। সত্যি কথা বলতে কী, এখনও এত স্পষ্ট সব কিছু মনে আছে দেখে আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। আরও বিশেষ করে, কারণ আমাকে তো আসলে শাস্তি দেওয়ার জন্য পাঠানো হয়েছিল এখানে।”
“কেন আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছেন?”
কাধ ঝাঁকাল কানাই। “আমি আসলে যে ধরনের মানুষ তাতে আমার পক্ষে এটা ঠিক স্বাভাবিক নয়। আমি অতীত আঁকড়ে পড়ে থাকি না। সব সময় সামনের দিকে তাকিয়ে চলতে পছন্দ করি।”
“কিন্তু এখানে, এই লুসিবাড়িতে এখন তো আমরা অতীতে নেই, আমরা তো বর্তমানে আছি, তাই না?” হেসে বলল পিয়া।
“মোটেও না,” জোর দিয়ে বলল কানাই। “আমার কাছে লুসিবাড়ি সবসময় অতীতেরই অংশ হয়ে থাকবে।”
ভাত শেষ হয়ে গিয়েছিল পিয়ার, টেবিল থেকে উঠে থালা বাসনগুলো গুছোতে শুরু করল ও। তাই দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠল কানাই।
“আরে, বসে পড়ুন। আপনি আবার এগুলোতে কেন হাত দিচ্ছেন? ওসব ময়না করে নেবে এখন।”
“আমি ময়নার থেকে কিছু খারাপ করব না,” পিয়া জবাব দিল।
কানাই কাঁধ ঝাঁকাল। “বেশ।”
নিজের প্লেটটা ধুতে ধুতে পিয়া বলল, “এই যে আপনি এখানে আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করলেন, এত কিছু করলেন, কিন্তু আমার এদিকে মনে হচ্ছে আমি তো আপনার সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানি না বলতে গেলে। শুধু নামটা ছাড়া।”
“তাই?” একটু অবাক হয়ে হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল কানাই। “কেমন করে ঘটল। এই আশ্চর্য ঘটনাটা বলুন তো? আমার খুব একটা বাক্ সংযম আছে বলে তো বাজারে কোনও দুর্নাম নেই।”
“তা হলেও, কথাটা সত্যি। এমনকী আপনি কোথায় থাকেন সেটা পর্যন্ত আমি জানি না।”
“এক্ষুনি সব সমস্যার সমাধান করে দিচ্ছি,” কানাই বলল। “আমি থাকি নতুন দিল্লিতে, আমার বয়স বিয়াল্লিশ এবং বেশিরভাগ সময়েই আমি সঙ্গিনীহীন।”
“তাই বুঝি?” একটু কম ব্যক্তিগত দিকে কথা ঘোরাল পিয়া, “আর আপনি তো ট্রান্সলেটর, তাই না? এই একটা কথা বলেছিলেন মনে আছে আমার।”
“একদম ঠিক। মৌখিক এবং লিখিত অনুবাদের কাজ করি আমি। যদিও এখন সেসব কিছুর চেয়ে ব্যবসাটাই বেশি করে করছি। বছর কয়েক আগে আমি খেয়াল করি যে দিল্লিতে পেশাদার ভাষাবিদের সংখ্যা খুব কম। তখন নিজেই একটা অফিস খুলে বসলাম। এখন আমার কোম্পানি সমস্ত রকম সংস্থার জন্য সব রকমের অনুবাদের কাজ করে–ব্যবসায়ীদের জন্য, বিভিন্ন দূতাবাসের জন্য, সংবাদমাধ্যমের জন্য, নানারকম সব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের জন্য–এক কথায়, যারাই পয়সা দেয় তাদেরই জন্য কাজ করি আমরা।”
“এ কাজের চাহিদা কী রকম বাজারে?”
“চাহিদা আছে, চাহিদা আছে,” মাথা নেড়ে বলল কানাই। “দিল্লি এখন হল পৃথিবীর ব্যস্ততম কনফারেন্স সিটিগুলির মধ্যে একটা। মিডিয়ারও প্রচুর কাজ। কিছু না কিছু একটা সব সময় লেগেই আছে। আমি তো কাজ করে কুলিয়ে উঠতে পারি না অনেক সময়। ব্যবসা সমানে বেড়েই যাচ্ছে। এই তো কয়েকদিন আগেই আমরা চালু করলাম একটা স্পিচ ট্রেনিং অপারেশন। কল সেন্টারে যারা কাজ করে তাদের ইংরেজি উচ্চারণ শেখানোর জন্য। সেই বিভাগের কাজ তো এখন দিনে দিনে বাড়ছে।”
শুধু মাত্র ভাষার আদান প্রদানের ওপর নির্ভর করে যে একটা ব্যবসা দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায় এই ধারণাটাই খুব আশ্চর্য মনে হল পিয়ার। “তা হলে আপনি নিজেও নিশ্চয়ই
অনেকগুলো ভাষা জানেন, তাই না?”
“ছ’টা,” মুচকি হেসে সঙ্গে সঙ্গে বলল কানাই। “হিন্দি, উর্দু আর বাংলাটাই প্রধানত কাজে লাগে এখন। আর ইংরেজি তো আছেই। তা ছাড়াও আরও দুটো জানি, ফরাসি আর আরবি–সেগুলোও সময়ে অসময়ে কাজে লেগে যায়।”
অদ্ভুত লাগল পিয়ার এই দুটো ভাষার কথা শুনে। “ফরাসি আর আরবি! এই ভাষাগুলো আবার কী করে শিখলেন?”
“স্কলারশিপ,” একটু হেসে বলল কানাই। “বিভিন্ন সব ভাষার ব্যাপারে আমার সব সময়ই খুব আগ্রহ। ছাত্র অবস্থায় প্রায়ই ঢু মারতাম কলকাতার অলিয়স ফ্রঁসেতে। তারপর এটা ওটা নানা যোগাযোগে স্কলারশিপ পেয়ে গেলাম একটা। তারপর প্যারিসে যখন ছিলাম সেই সময় একটা সুযোগ এল টিউনিশিয়াতে গিয়ে আরবি শেখার। এরকম সুযোগ আর কে ছাড়ে? তারপর থেকে আর কখনও পেছনে তাকাতে হয়নি।”
একটা হাত তুলে ডান কানের রুপোর দুলটা খুঁটতে লাগল পিয়া। ভঙ্গিটার আত্মবিস্মৃত ভাবটা ছেলেমানুষি, কিন্তু তারই মধ্যে যুবতীসুলভ একটা সুষমাও রয়েছে। “আপনি তা হলে ঠিকই করে নিয়েছিলেন যে এই অনুবাদের কাজটাকেই এক সময় পেশা করবেন?”
“না না,” বলল কানাই। “একেবারেই না। আমি যখন আপনার বয়সি ছিলাম, কলকাতার আর পাঁচটা কলেজের ছাত্রর মতো তখন আমারও মাথার মধ্যে গজগজ করত কবিতার ভূত। পেশাদারি জীবনের শুরুতে আমার ইচ্ছে ছিল আমি জীবনানন্দ অনুবাদ করব আরবিতে আর অ্যাডোনিস অনুবাদ করব বাংলায়।”
“তারপর কী হল?” নাটকীয় ভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল কানাই। “সংক্ষেপে বলতে গেলে, কিছুদিনের মধ্যেই আমি আবিষ্কার করলাম যে ভাষা হিসেবে যদিও বাংলা এবং আরবি দুটোরই সম্পদ অপরিমেয়, কিন্তু এই দুটোর কোনও ভাষাতেই শুধু সাহিত্যিক অনুবাদের কাজ করে পেট চালানো সম্ভব নয়। বড়লোক আরবদের বাংলা সাহিত্যের বিষয়ে কোনও আগ্রহই নেই, আর বড়লোক বাঙালিদের কীসে আগ্রহ আছে তাতে কিছুই যায় আসে না, কারণ সংখ্যায় তারা এত কম যে তাদের পক্ষে কিছু করে ওঠা সম্ভব নয়। একটা সময় এসে তাই আমি নিজেকে ভাগ্যের হাতে সঁপে দিলাম, আর এইসব ব্যবসায়িক কাজ শুরু করলাম। তবে এটা বলতেই হবে খুবই ভাল সময়ে শুরু করেছি আমি : অনেক কিছু হচ্ছে এখন এই দেশে, আর তার অংশ হতে পারাটা বেশ একটা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা আমার মনে হয়।”
পিয়ার মনে পড়ল বাবার কাছে শোনা ইন্ডিয়ার গল্প, যে দেশ ছেড়ে বাবা চলে গিয়েছিল আমেরিকায় : সে ছিল এমন এক দেশ যেখানে গাড়ি ছিল মাত্র দু’রকমের, আর যেখানে মধ্যবিত্ত জীবনকাঠামোর প্রধান ধর্ম ছিল বিদেশি যে-কোনও কিছুর প্রতি এক তীব্র আকর্ষণ। কিন্তু কানাই যে জগতে বাস করে এই লুসিবাড়ি বা ভাটির দেশের থেকে সে পৃথিবী যতটা দূরে, পিয়ার বাবার স্মৃতির ভারতের সঙ্গে তার দূরত্ব কোনও অংশে কম নয়।
“আপনার কখনও আবার সাহিত্যিক অনুবাদের কাজে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে হয় না?” ও জিজ্ঞেস করল কানাইকে।
“হয় কখনও কখনও। খুব বেশি হয় না। সব মিলিয়ে এটা স্বীকার করতেই হবে যে একটা গোটা অফিস চালাতে আমার বেশ ভালই লাগে। ভাবতে ভাল লাগে আমি লোকজনদের চাকরি দিচ্ছি, মাইনে দিচ্ছি, অর্থহীন ডিগ্রিওয়ালা ছাত্রছাত্রীদের কাজের সুযোগ করে দিচ্ছি। আর, পয়সা এবং স্বাচ্ছন্দ্যটাও যথেষ্ট উপভোগ করি আমি। সেটা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। পয়সাওয়ালা একা লোকের পক্ষে দিল্লি বেশ ভাল জায়গা। অনেক ইন্টারেস্টিং মহিলার সঙ্গে যোগাযোগ হয়।”
এই শেষ কথাটায় একেবারে আশ্চর্য হয়ে গেল পিয়া। এক মুহূর্ত ঠিক বুঝে উঠতে পারল
কী বলবে। বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে সদ্য বোয়া প্লেটগুলোকে গুছিয়ে রাখছিল ও। শেষ প্লেটটা রেখে একটা হাই তুলল, এক হাত তুলে আড়াল করল মুখটা।
“সরি।”
সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে কানাই বলল, “এত সব ঘটনার পরে নিশ্চয়ই খুব টায়ার্ড আপনি?”
“ভীষণ। মনে হচ্ছে ঘুমোতে যেতে হবে এবার।”
“এক্ষুনি?” জোর করে একটু হাসল কানাই, যদিও বোঝাই যাচ্ছিল বেশ একটু হতাশ হয়েছে ও। “অবশ্য ঠিকই তো, যা ধকলটা গেছে। আপনাকে বলেছি কি যে আর ঘণ্টাখানেক বাদে কিন্তু ইলেকট্রিক আলো বন্ধ হয়ে যাবে। হাতের কাছে মোমবাতি রাখবেন একটা।”
“তার অনেক আগেই আমি ঘুমিয়ে পড়ব।”
“গুড। আশা করি ভাল করে বিশ্রাম নিতে পারবেন রাত্তিরটা। আর যদি কিছু দরকার হয়, ওপরে গিয়ে দরজা ধাক্কাবেন। আমি মেসোর পড়ার ঘরে থাকব।”
.
ঝড়
পরের সপ্তাহেই আবার মরিচঝাঁপি যাব ঠিক করেছিলাম, কিন্তু হেডমাস্টারের রিটায়ার করার সময় অনেক টুকিটাকি কাজ আর নিয়মমাফিক অনুষ্ঠান থাকে–সেই সবের মধ্যে আটকে গেলাম আমি। অবশেষে সব ঝামেলা মিটল, সরকারিভাবে শেষ হয়ে গেল আমার কর্মজীবন।
কয়েকদিন পর আমার পড়ার ঘরে এসে কড়া নাড়ল হরেন। “সার!”
“কুমিরমারির বাজারে গিয়েছিলাম,” ও বলল। “সেখানে কুসুমের সঙ্গে দেখা। ও কিছুতেই ছাড়বে না, বলল ওকে এখানে নিয়ে আসতে হবে।”
“এখানে!” প্রায় চমকে উঠলাম আমি। “এই লুসিবাড়িতে? কেন?”
“ও মাসিমার সঙ্গে দেখা করবে। মরিচঝাঁপির লোকেরা মাসিমার সাহায্য চায়।”
সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম আমি। এটাও স্থানীয় সমর্থন জোগাড়ের জন্য উদ্বাস্তুদের চেষ্টার অঙ্গ। তবে এই ক্ষেত্রে ওদের চেষ্টায় কোনও ফল হবে বলে মনে হল না আমার।
“হরেন, তুমি কুসুমকে বারণ করতে পারতে,” বললাম আমি। “নীলিমার সঙ্গে দেখা করে ওদের কোনও লাভ হবে না।”
“বলেছিলাম সার। কিন্তু ও কিছুতেই ছাড়বে না।”
“ও কোথায় এখন?”
“নীচে সার। মাসিমার জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু আপনার কাছে কাকে নিয়ে এসেছি দেখুন।” একপাশে সরে দাঁড়াল হরেন, আর আমি দেখলাম এতক্ষণ ধরে ওর আড়ালে লুকিয়ে দাঁড়িয়েছিল ফকির।
“আমাকে একবার বাজারে যেতে হবে। ওকে তাই আপনার কাছে রেখে গেলাম।” পাঁচ বছরের ছেলেটাকে আমার কাছে বসিয়ে রেখে একদৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে গেল ও।
এতদিন মাস্টারি করতে করতে একাধিক বাচ্চার সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করতে হয় সেটাই জেনেছি, কিন্তু নিজের কোনও সন্তান না থাকায়, শুধুমাত্র একজন শিশুর সাথে কথা বলার অভ্যাস আমার ছিল না। এখন একজোড়া পাঁচ বছর বয়সি খোলা চোখের নজরের সামনে বসে আমি যা যা বলব ভেবে রেখেছিলাম সবই ভুলে গেলাম।
প্রায় আতঙ্কে ছেলেটাকে নিয়ে ছাদের ধারে গেলাম আমি। সামনে রায়মঙ্গলের মোহনার দিকে দেখিয়ে বললাম, “দেখো কমরেড, সামনে চোখ মেলে তাকাও, বলো আমাকে কী দেখতে পাচ্ছ।”
মনে হল আমি কী জানতে চাইছি সেটা নিজেকেই ও মনে মনে জিজ্ঞেস করছিল। খানিক এদিক ওদিক তাকিয়ে অবশেষে বলল, “বাঁধ দেখতে পাচ্ছি সার।”
“বাঁধ দেখতে পাচ্ছ? তা তো বটেই, বাঁধই তো দেখা যাচ্ছে।”
এই উত্তর আমি আদৌ আশা করিনি, কিন্তু খুবই স্বস্তি পেলাম মনে মনে জবাবটা পেয়ে। কারণ এই ভাটির দেশে বাঁধ শুধু যে মানুষের প্রাণরক্ষা করে তা তো নয়, বাঁধই তো আমাদের ইতিহাসের ভাড়ারঘর, অঙ্কের আকর, গল্পের খনি। এই বাঁধ যতক্ষণ আমার চোখের সামনে আছে, আমি জানি আমার কথা বলার বিষয়ের কোনও অভাব হবে না।
“ঠিক আছে কমরেড, চালিয়ে যাও। আবার দেখো, খুব ভাল করে দেখো। দেখি তো খুঁজে বের করতে পারো কিনা কোন কোন জায়গায় বাঁধটা সারাই করা হয়েছে। প্রত্যেকটা জায়গার জন্য আমি একটা করে গল্প বলব তোমাকে।”
হাত তুলে একটা জায়গার দিকে ইশারা করল ফকির। “ওইখানটায় কী হয়েছিল সার?”
“আচ্ছা, ওইখানটায়। কুড়ি বছর আগে ওই জায়গায় বাঁধটা ভেঙেছিল। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, ঝড়েও ভাঙেনি, কন্যাতেও ভাঙেনি। একটা লোক গিয়ে ওখানে বাঁধটা কেটে দিয়েছিল। কেন জানো? এক পড়শির সঙ্গে ওর ঝগড়া হয়েছিল, সেইজন্য। রাতের অন্ধকারে চুপিচুপি গিয়ে বাঁধের ওই জায়গাটায় ও একটা গর্ত করে রেখে এল। ভাবল ওখান দিয়ে নোনা জল ঢুকে পড়শির খেতটা ডুবিয়ে দেবে। কিন্তু এটা ওর মাথায় আসেনি যে বাঁধ কেটে ও নিজেরও একই ক্ষতি করছে। তাই ওদের দু’জনের কেউই আর এখন এখানে থাকে না কারণ নোনা জল ঢোকার পর দশ বছর পর্যন্ত আর কিছু চাষ করা যায়নি ওই জায়গার জমিতে।”
“আর ওখানটায় সার? ওখানে কী হয়েছিল?”
“ওই জায়গার গল্পটা শুরু হয়েছিল একবার জোয়ারের সময়। কোটাল গোনে জল খুব বেড়ে গিয়েছিল সেবার, তারপরে ওখান দিয়ে উপছে এসে ঢুকেছিল গাঁয়ে। তখন বাঁধ সারাইয়ের ঠিকাদারি যাকে দেওয়া হল সে ছিল তখনকার গ্রামপ্রধানের শালা। সে তো বলল এমন করে সারিয়ে দেবে যে জীবনে আর জল ঢুকবে না ওখান দিয়ে। কিন্তু পরে দেখা গেল ও জায়গায় যত মাটি ফেলার পয়সা তাকে দেওয়া হয়েছিল তার মাত্র অর্ধেক পয়সার মাটি ফেলেছে। বাকি পয়সাটা অন্যসব শালাদের সঙ্গে ভাগ করে খেয়ে ফেলেছে।”
“আর ওই জায়গাটায় সার?”
ভাল গল্প বলিয়েদেরও মাঝে মাঝে থামতে জানতে হয়। জানতে হয় কখনও কখনও বিচক্ষণতার দাম সাহসের চেয়ে অনেক বেশি। “ওই জায়গাটার বিষয়ে কমরেড খুব বেশি কিছু আমি তোমাকে বলতে পারব না। ওখানে যারা থাকে তাদের দেখতে পাচ্ছ, ওই যে বাঁধের ধার ঘেঁষে পরপর ঘরগুলোতে? এখন ব্যাপার হল গিয়ে একবার ওই লোকগুলো একটা ভুল দলকে ভোট দিয়ে ফেলেছিল। ফলে অন্য আরেক পার্টি যখন ক্ষমতায় এল, তারা ঠিক করল শোধ নিতে হবে। সেই শোধ নেওয়ার জন্য ওরা কী করল? না, ওই জায়গায় বাঁধের গায়ে একটা গর্ত করে রেখে দিল। রাজনীতি যারা করে তারা এইরকমই হয়, তবে এই নিয়ে আর বেশি কথা না বলাই ভাল–এই বিষয়টা আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব একটা ভাল নাও হতে পারে। তার চেয়ে বরং ওই জায়গাটা দেখো, ওই যে, আমি আঙুল দিয়ে য়ে জায়গাটা দেখাচ্ছি, ওইখানটা।”
যে জায়গাটার দিকে আমি ইশারা করলাম তিরিশের দশকের এক ঝড়ে সেখানে প্রায় কিলোমিটারখানেক বাঁধ ভেঙে বেরিয়ে গিয়েছিল।
“একবার কল্পনা করো ফকির, কী কঠিন জীবন ছিল তোমার পূর্বপুরুষদের,” বললাম আমি। “ওরা তখন মাত্রই এসেছে এই ভাটির দেশে, নতুন এসে বসত করেছে এই দ্বীপে। বছরের পর বছর ধরে নদীর সাথে লড়াই করে আস্তে আস্তে এই বাঁধের ভিতটা সবে বানিয়েছে। বহু পরিশ্রমে কয়েক মুঠো ধান আর আলুপটলও ফলাতে পেরেছে। বছরের পর বছর খুঁটির ওপর বাসা বানিয়ে থাকার পর অবশেষে নেমে আসতে পেরেছে মাটিতে। সমান জমিতে কয়েকটা বস্তি ঝুপড়ি বানাতে পেরেছে। এই সবকিছুই কিন্তু ওই বাঁধের কল্যাণে। এবার কল্পনা করো সেই ভয়াবহ রাতের কথা। ঝড় যখন এল তখন সবে কোটাল লেগেছে; ভাবো একবার, সেই চাল-উড়ে যাওয়া ঘরে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসে বসে ওরা দেখছে জল বাড়ছে, বাড়ছে… এত বছরের পরিশ্রমে নদীকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য যে বালি আর মাটি জড়ো করেছিল ওরা, চোখের সামনে তার ওপর এসে আছড়ে আছড়ে পড়ছে ঢেউ। ভাবো একবার, কীরকম লাগছিল ওরা যখন দেখল মাটি গলিয়ে হু হু করে ঢুকে আসছে জোয়ারের জল, তাড়া করে আসছে পেছন পেছন, পালিয়ে বাঁচার কোনও উপায়ই নেই। আমি তোমাকে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি দোস্ত, সেদিন এই নদীর সামনে দাঁড়িয়ে ওই দৃশ্য দেখার চেয়ে বাঘের মুখে গিয়ে দাঁড়াতে বললেও রাজি হয়ে যেত ওদের যে কেউ।”
“আরও ঝড় হয়েছিল সার?”
“আরও অনেকবার ঝড় এসেছে ফকির, অনেকবার। দেখো ওই জায়গাটার দিকে তাকিয়ে দেখো,” নদীর পাড়ে দ্বীপের একটা জায়গার দিকে দেখালাম আমি। দেখে মনে হয় যেন বিশাল কোনও দানব কোনওদিন লুসিবাড়ির নদীতীরের ওই জায়গা থেকে একটা টুকরো কামড়ে ছিঁড়ে নিয়েছে। “দেখো। ১৯৭০ সালের ঝড়ে এই কাণ্ড হয়েছিল। বিশাল ভাঙন ধরেছিল–দ্বীপের চার একর জমি ওখান থেকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছিল নদী। মুহূর্তের মধ্যে মাঠ ঘাট গাছপালা বাড়িঘর সবসুদ্ধ চলে গেল জলের তলায়।”
“সবচেয়ে বড় ঝড় ছিল ওটা?”
“না কমরেড, না। সবচেয়ে বড় ঝড় যেটাকে বলা হয়, সে হয়েছিল আমারও জন্মের আগে। এখানে লোকজন এসে বসত শুরু করারও অনেক আগে।”
“কবে সার?”
“সে ঝড় হয়েছিল ১৭৩৭ সালে। তার তিরিশ বছর আগে ঔরঙ্গজেব বাদশা মারা গেছেন, সারা দেশ জুড়ে নানা গোলমাল। কলকাতা শহরের সবে জন্ম হয়েছে। গোলমালের সুযোগ নিয়ে ইংরেজরা এসে আস্তে আস্তে উঁকিয়ে বসছে। এই গোটা পুবদেশে তখন কলকাতা তাদের প্রধান বন্দর।”
“তারপর কী হল সার?”
“সে ঝড় হয়েছিল অক্টোবর মাসে। ওই সময়টাতেই বেশি ঝড় হয়–অক্টোবর আর নভেম্বর। সে ঝড়ের ঘা এসে লাগার আগেই বিশাল এক ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল এই ভাটির দেশে। বারো মিটার উঁচু সেই জলের দেওয়াল এসে ভেঙে পড়ল এখানে। কত বড় ঢেউ বুঝতে পারছ? ওইরকম একটা ঢেউ যদি এখন আসে, তা হলে তোমার দ্বীপ তো বটেই, আমাদের এই দ্বীপেও সবকিছু জলের তলায় চলে যাবে। এই ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে থাকলেও ডুবে যাব আমরা।”
“না।”
“হ্যাঁ, কমরেড, হ্যাঁ। কলকাতার কিছু ইংরেজ তখন এইসব মাপজোক করে সমস্ত লিখে রেখে দিয়েছিল। এতদূর পর্যন্ত জল উঠেছিল যে হাজার হাজার জন্তু জানোয়ার মারা পড়েছিল তাতে। সেই মরা জানোয়ারগুলো জলের টানে নদীর উজান বরাবর বহু দূর পর্যন্ত ভেসে গিয়েছিল। অনেক জায়গায় ডাঙার ভেতরে পর্যন্ত চলে গিয়েছিল সেইসব জীবজন্তুর লাশ। এমনকী নদী থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে ধানজমিতে, গ্রামের পুকুরের মধ্যে মরা বাঘ আর গণ্ডারের দেহ পাওয়া গিয়েছিল সেই ঝড়ের পরে। মাঠের পর মাঠ ছেয়ে গিয়েছিল মরা পাখির পালকে। আর সেই ঢেউ যখন এই ভাটির দেশের ওপর দিয়ে কলকাতার দিকে ধেয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময় আরও একটা ঘটনা ঘটল–এক অকল্পনীয় ঘটনা।”
“কী ঘটল সার? কী ঘটল?”
“বিরাট এক ভুমিকম্প হল কলকাতায়।”
“সত্যি সত্যি?”
“সত্যি, দোস্ত। একেবারে খাঁটি সত্যি। সেই জন্যেই আরও এই ঝড়ের কথা মনে আছে লোকের। কোনও কোনও বৈজ্ঞানিকের ধারণা যে ঝড় আর ভূমিকম্পের মধ্যে কোনও একটা রহস্যজনক সম্পর্ক আছে। কিন্তু এই প্রথম দুটোই একসঙ্গে ঘটতে দেখা গেল।”
“তারপরে কী হল সার?”
“মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার বাড়ি ধসে পড়ল কলকাতায়। ইংরেজদের প্রাসাদ থেকে শুরু করে এমনি সাধারণ বাড়ি, কুঁড়েঘর, কিছুই রেহাই পেল না। ইংরেজদের যে গির্জা ছিল, তার চুড়োটা টুকরো টুকরো হয়ে এসে পড়ল মাটিতে। লোকে বলে শহরের একটা বাড়িরও নাকি চারটে গোটা দেওয়াল অক্ষত ছিল না। সেতু-টেতু সব উড়ে চলে গেল, জাহাজঘাটাগুলো জলের তোড়ে কোথায় ভেসে গেল, গুদামের ধানচাল কিচ্ছু বাকি রইল না, বারুদখানার বারুদও হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। দেশ-বিদেশের ছোটবড় জাহাজ সব নোঙর করা ছিল তখন নদীতে। তার মধ্যে ইংরেজদেরও দুটো জাহাজ ছিল–পাঁচশো টনের জাহাজ একেকটা। সেই জাহাজগুলোকে জল থেকে তুলে উড়িয়ে নিয়ে গেল ঝড়ে, গাছপালা ঘরবাড়ির ওপর দিয়ে উড়ে নদী থেকে আধ কিলোমিটার দূরে গিয়ে পড়ল সেগুলো। বিশাল বিশাল সব বজরা কাগজের ঘুড়ির মতো লাট খেতে খেতে উড়ে গেল। শোনা যায় সবসুদ্ধ কুড়ি হাজার জাহাজ, নৌকো, বজরা আর ডিঙি নষ্ট হয়েছিল ওই একদিনে। যেগুলো টিকে ছিল, সেগুলি নিয়েও অদ্ভুত সব ঘটনার কথা শোনা যেতে লাগল।”
“কীরকম ঘটনা সার?”
“একটা ফরাসি জাহাজ ঝড়ের তোড়ে পাড়ের ওপর অনেকটা দূর পর্যন্ত উঠে গিয়েছিল। কিন্তু জাহাজের মালপত্র সব নষ্ট হয়নি। ঝড়ের পরদিন, জাহাজের নাবিকদের মধ্যে যে ক’জন বেঁচেছিল তারা মাঠের মধ্যে দেখতে গেল–ওই ধ্বংসাবশেষ থেকে যদি কিছু উদ্ধার করা যায়। একজন মাল্লাকে পাঠানো হল জাহাজের খোলের ভেতর কী কী অক্ষত আছে গিয়ে দেখে আসতে। তারপর বেশ খানিকক্ষণ কেটে গেল, কিন্তু লোকটা আর বেরোয় না। বাইরে যারা ছিল, তারা চেঁচিয়ে ডাকাডাকি করতে লাগল, কিন্তু কোনও সাড়া নেই। তখন আরেকজন লোককে পাঠানো হল। খোলের ভেতরে ঢুকে যাওয়ার পর তার কাছ থেকেও কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। তারপর আরও একটা লোক গেল, কিন্তু সেই একই ব্যাপার। বাইরে যারা ছিল তারা তখন খুব ভয় পেয়ে গেল। কেউ আর খোলের মধ্যে ঢুকতে রাজি হয় না। শেষে একটা আগুন জ্বালানো হল–অন্ধকার খোলের ভিতরে কী ব্যাপারটা হচ্ছে সেটা দেখার জন্য। আগুন যখন দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করল, সেই আলোয় দেখা গেল খোলের ভেতরটা জলে টইটম্বুর, আর তার মধ্যে সাঁতরে বেড়াচ্ছে এক প্রকাণ্ড কুমির। ওই তিনটে লোককে সেটাই মেরে ফেলেছে।
“এটা কিন্তু বানানো গল্প নয় কমরেড, এক্কেবারে খাঁটি সত্যি ঘটনা। এই সমস্ত বিবরণ লেখা নথিপত্র যত্ন করে রাখা আছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে, যেখানে বসে দাস ক্যাপিটাল লিখেছিলেন মার্ক্স সাহেব।”
“ওরকম ঝড় তো আর হবে না, তাই না সার?”
বুঝতে পারলাম আমাদের এইসব নদীর খিদে কতটা হতে পারে সেটা আঁচ করার চেষ্টা করছে ফকির। ওর ছোট্ট মনটাকে শান্তি দিতে পারলে খুশি হতাম, কিন্তু সেরকম ছলনা করতে মন চাইল না। “সে কথা বলা যায় না বন্ধু। সত্যি কথা বলতে কী, ওরকম আবার ঘটবে। ঘটবেই। প্রচণ্ড ঝড় আসবে, ফুঁসে উঠবে নদী, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে বাঁধ। এ শুধু সময়ের অপেক্ষা।”
“কী করে জানলেন সার?” মিনমিন করে জিজ্ঞেস করল ফকির।
“দেখো দোস্ত, সামনের দিকে চেয়ে দেখো। দেখো কত দুর্বল, পলকা আমাদের এই বাঁধ। এবার তার ওপারে জলের দিকে দেখো–দেখো কী বিপুল তার বিস্তার, কেমন ধীর শান্তভাবে বয়ে চলেছে। শুধু তাকিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে, আজ হোক কি কাল হোক, এই লড়াইয়ে নদীরই জয় হবে একদিন। কিন্তু শুধু চোখে দেখে যদি বিশ্বাস না হয়, তা হলে তোমাকে ভরসা করতে হবে তোমার কানের ওপর।”
“আমার কান?”
“হ্যাঁ। এসো আমার সঙ্গে।”
সিঁড়ি দিয়ে নেমে মাঠের ওপারে চললাম আমরা। লোকজন নিশ্চয়ই টেরিয়ে টেরিয়ে দেখছিল আমাদের দিকে এক লতপতে ধুতি পরে আমি চলেছি, রোদ আটকানোর জন্য ছাতা খুলে ধরেছি মাথায়, আর ছোট্ট ফকির ছেঁড়া হাফপ্যান্ট পরে আমার পায়ে পায়ে দৌড়ে চলেছে। সোজা বাঁধের কাছে গিয়ে আমার বাঁ কানটা মাটিতে চেপে ধরলাম আমি। “বাঁধের ওপর কান পাতো, তারপর মন দিয়ে শোনো। দেখি বুঝতে পারো কি না কী হচ্ছে।”
খানিক পরে ফকির বলল, “একটা আঁচড় কাটার শব্দ শুনতে পাচ্ছি সার। খুব আস্তে আস্তে হচ্ছে শব্দটা।”
“কিন্তু কীসের ওই শব্দটা?”
আরও খানিকক্ষণ কান পেতে শুনল ফকির। তারপর একটা হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর মুখ। “কাঁকড়া, তাই না সার?”
“ঠিক ধরেছ ফকির। সবাই শুনতে পায় না ওই আওয়াজ, কিন্তু তুমি পেলে। অগুন্তি কাঁকড়া দিনরাত কুরে কুরে গর্ত করে চলেছে আমাদের এই বাঁধের ভেতর। এখন ভাবো এইসব কাঁকড়া আর জোয়ার, বাতাস আর ঝড়ের রাক্ষুসে খিদের সঙ্গে কতদিন পাল্লা দিতে পারবে আমাদের এই ঠুনকো মাটির বাঁধ? আর যখন এই বাঁধ ভেঙে যাবে তখন কার কাছে গিয়ে দাঁড়াব আমরা, কমরেড?”
“কার কাছে, সার?”
“কার কাছে? দেবদূতরাও না, মানুষও না, কেউই আমাদের ডাক শুনতে পাবে না সেদিন। আর জন্তু জানোয়ারদের কথা যদি বলো, তারাও শুনবে না আমাদের কথা।”
“কেন শুনবে না সার?”
“কারণটা কবি লিখে গেছেন, ফকির। কারণ ওই পশুরাও
‘জেনে গেছে, এই
ব্যাখ্যাত জগতে নেই আমাদের স্বাচ্ছন্দ্য বা
স্থিতিবোধ।”
.
আলোচনা
লুসিবাড়ি হাসপাতালের ট্রেনি নার্সদের জন্যও স্টাফ কোয়ার্টার্সের ব্যবস্থা আছে। ময়না সেখানেই থাকে। বাঁধের পাশেই একটা টানা লম্বা ব্যারাকের মতো বাড়িতে পরপর সব কোয়ার্টার্স। ট্রাস্টের সীমানার একপ্রান্তে মিনিট পাঁচেক লাগে গেস্ট হাউস থেকে হেঁটে যেতে।
বাড়িটার একেবারে শেষে ময়নার কোয়ার্টার্স। একটা বড় ঘর আর এক টুকরো উঠোন। দরজায় দাঁড়িয়ে কানাই আর পিয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল ময়না। সামনে যেতে হেসে নমস্কার করল হাতজোড় করে। তারপর উঠোনটার মধ্যে নিয়ে গেল ওদের। কয়েকটা ফোল্ডিং চেয়ার রাখা সেখানে ওদের জন্য।
একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে চারিদিকে একবার তাকাল পিয়া। “টুটুল কোথায়?”
“স্কুলে,” ময়নার কাছ থেকে জেনে নিয়ে বলল কানাই।
“আর ফকির?”
“ওই যে, ওখানে।”
মাথা ঘুরিয়ে পিয়া দেখল ঘরের দরজার সামনেটায় উবু হয়ে বসে আছে ফকির। একটা তেলচিটে নীল পর্দায় আড়াল পড়ে গেছে খানিকটা। একবার মুখ তুলে তাকালও না ও। এমনকী চিনতে যে পেরেছে সেরকমও মনে হল না ওর হাবভাব দেখে। মাটির দিকে তাকিয়ে বসে বসে একটা কাঠি দিয়ে নকশা আঁকতেই লাগল। পরনে সেই একটা টি-শার্ট আর লুঙ্গি; কিন্তু ডিঙিতে দেখে যেটা মনে হয়নি, এখানে ওরই নিজের বাড়ির এই পরিবেশের মধ্যে সেগুলিকে কেমন রং-জ্বলা হতদরিদ্র চেহারার মনে হল পিয়ার। এমন একটা এড়িয়ে-যাওয়া গোমড়ানো ভাব নিয়ে বসেছিল ফকির যে মনে হল প্রচণ্ড চাপে পড়ে (ময়নার না প্রতিবেশীদের?) আজকে এখানে উপস্থিত থাকতে রাজি হয়েছে ও।
ফকিরের এই পরাজিত ভীত চেহারাটা বুকে শেলের মতো বিধল পিয়ার। যে লোকটা ওর প্রাণ বাঁচানোর জন্য এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিল তার আবার কীসের ভয়? পিয়ার ইচ্ছে করছিল ফকিরের সামনে গিয়ে সোজা ওর চোখের দিকে তাকিয়ে সহজ স্বাভাবিকভাবে কথা বলে ওর সঙ্গে। কিন্তু ওর ভঙ্গি দেখে মনে হল এখানে, ময়না আর কানাইয়ের উপস্থিতিতে, সেটা করলে ওর অস্বস্তি বাড়বে বই কমবে না।
কানাইও দেখছিল ফকিরকে। একান্তে ফিসফিস করে পিয়াকে বলল, “আমি ভেবেছিলাম শুধু টিয়াপাখিই ওইভাবে বসতে পারে।”
তখন পিয়া নজর করল, ও যেরকম ভেবেছিল সেরকম মেঝের ওপর বসে নেই ফকির, দরজার চৌকাঠটার ওপর উবু হয়ে বসে আছে ও, আর পাখি যেমন দাড়ের ওপর বসে, সেইভাবে পায়ের আঙুল দিয়ে আঁকড়ে রেখেছে কাঠটাকে।
ওদের কথাবার্তায় ফকিরের বিন্দুমাত্রও আগ্রহ নেই দেখে অবশেষে পিয়া ঠিক করল ওর বউয়ের সঙ্গেই কথা বলবে ও। কানাইকে জিজ্ঞেস করল, “আমার জন্য একটু দোভাষীর কাজ করে দেবেন প্লিজ?”
কানাইয়ের মাধ্যমেই পিয়া ময়নাকে তার কৃতজ্ঞতা জানাল, তারপর বলল ফকির ওর জন্য যা করেছে তার জন্য ফকিরের পরিবারকে ও সামান্য কিছু উপহার দিতে চায়।
আগে থেকেই একতোড়া নোট গুছিয়ে নিয়ে এসেছিল পিয়া। বেল্টে বাঁধা ব্যাগ থেকে সেটা বের করতে করতে দেখল কানাই একটু পেছনে হেলে জায়গা করে দিচ্ছে, যাতে পাশের চেয়ার পর্যন্ত হাত বাড়িয়ে টাকাটা দিতে পারে পিয়া। ময়নাও একটা প্রত্যাশার হাসি মুখে নিয়ে একটু এগিয়ে বসেছে। বোঝাই যাচ্ছে ওরা দুজনেই আশা করে আছে পিয়া টাকাটা ময়নাকেই দেবে, ফকিরকে নয়। এক মুহূর্ত আগে পর্যন্ত পিয়াও সেরকমই ঠিক করেছিল, কিন্তু এখন টাকাটা হাতে নিয়ে ওর বিচারবুদ্ধি বিদ্রোহ করে উঠল–ওকে তো নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে জল থেকে টেনে তুলেছিল ফকির, কাজেই এই টাকা ফকিরের হাতে দেওয়াটাই যুক্তিযুক্ত হবে। ফকির ওর জন্য যা কিছু করেছে তার পরে পিয়া ওর সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে পারে না যাতে মনে হয় ফকিরের কোনও অস্তিত্বই নেই। টাকাটা নিয়ে ও বউকে দেবে কি বাড়ির জন্য খরচ করবে সেটা একান্তই ওর ব্যাপার–ওর হয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনও অধিকার তো পিয়ার নেই।
চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল পিয়া, কিন্তু ময়নাও চট করে উঠে এসে ওর সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল হাত পেতে। এইভাবে বাধা পাওয়ার পর তো পিয়ার আর কিছু করার থাকে না সেই অবস্থায় ওর পক্ষে যতটা সম্ভব শোভনভাবে ময়নার হাতেই টাকাটা তুলে দিল পিয়া।
“ময়না বলছে ওর স্বামীর তরফ থেকে এই উপহার নিয়ে ও খুব খুশি হয়েছে।”
পিয়া লক্ষ করল এই পুরো সময়টাই ফকির কিন্তু সেই একভাবে বসে রইল, একটুও নড়ল না–যেন এইভাবে অদৃশ্য মানুষের মতো থাকতেই ও অভ্যস্ত।
চেয়ারে ফিরে যেতে যেতে পিয়া শুনল ফকির কিছু একটা বলল, আর সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল ময়না।
“কী বলল ফকির?” ফিসফিস করে পিয়া জিজ্ঞেস করল কানাইকে।
“ও বলল এইরকম কিছুর জন্য টাকা নেওয়াটা ভাল দেখায় না।”
“আর ময়না কী জবাব দিল?”
“ময়না বলল, তা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই–ঘরে খাবার কিছু নেই, একটা পয়সাও নেই। শুধু কয়েকটা কাঁকড়া ছাড়া আর কিছু নেই।”
পিয়া কানাইয়ের মুখোমুখি ঘুরে বসে বলল, “দেখুন, ওদের স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে আমি নাক গলাতে চাই না, কিন্তু ব্যাপারটা শুধু আমার আর ময়নার মধ্যে থাকুক সেটাও চাই না আমি। ফকির কিছু বলে কিনা একটু দেখুন না। ওর সঙ্গেই কথা বলার দরকার আমার।”
“দেখি কী করতে পারি,” বলল কানাই। চেয়ার ছেড়ে উঠে ও ফকিরের সামনে গেল। তারপর খানিকটা বন্ধুত্বের সুরে সহৃদয় গলায় একটু জোরে বলল, “হ্যাঁ গো ফকির, আমাকে চেনো তুমি? আমি মাসিমার ভাগনে, কানাই দত্ত।”
কোনও জবাব দিল না ফকির। কানাই আবার বলল, “আমি তোমার মাকে চিনতাম, তুমি জানো?”
এই কথায় ঘাড় তুলে তাকাল ফকির। আর এই প্রথম সামনাসামনি ফকিরের মুখটা দেখে অবাক হয়ে গেল কানাই। কী আশ্চর্য মিল কুসুমের চেহারার সঙ্গে চোয়ালের গড়ন, একটু ভেতরে ঢোকা ঘোলাটে চোখ, এমনকী চুলের ধরনটা আর ভাবভঙ্গিও পুরো ওর মা-র মতো। কিন্তু কথাবার্তা বলার কোনও উৎসাহ ওর মধ্যে দেখা গেল না। এক মুহূর্ত কানাইয়ের চোখাচোখি তাকিয়ে আবার মুখ ঘুরিয়ে নিল ও, কোনও জবাব দিল না প্রশ্নের। কানাই কটমট করে ওর দিকে একটু চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে আবার নিজের জায়গায় ফিরে এল।
“কী হল?” জিজ্ঞেস করল পিয়া।
“চেষ্টা করছিলাম, যদি কথা বলানো যায়। বললাম আমি ওর মাকে চিনতাম।”
“ওর মাকে? আপনি চিনতেন?”
“চিনতাম,” বলল কানাই। “মারা গেছে ও। যখন ছেলেবেলায় এখানে এসেছিলাম তখন ওর মা-র সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার।”
“সেটা বললেন ওকে?”
“চেষ্টা করলাম,” একটু হাসল কানাই। “কিন্তু আমাকে কোনও পাত্তাই দিল না ও।”
মাথা নাড়ল পিয়া। ওদের দুজনের মধ্যে কথা কী হয়েছে সেটা ও বুঝতে পারেনি, কিন্তু ফকিরের সঙ্গে কথা বলার সময় কানাইয়ের গলার দাক্ষিণ্যের সুরটুকু পিয়ার কান এড়ায়নি। এমন সুরে কথা বলছিল ও, যেন কোনও হাবাগবা চাকর বাকরের সঙ্গে কথা বলছে–খানিকটা মশকরার সঙ্গে একটু কর্তৃত্ব মেশানো একটা অদ্ভুত সুর। ফকির যে চুপ করেছিল তাতে একটুও অবাক হয়নি পিয়া–ওটাই ওর স্বাভাবিক আত্মরক্ষার কৌশল।
“যাক, ওকে আর ঘটানোর দরকার নেই, আমরা বরং এবার উঠি,” পিয়া বলল।
“আমি তো রেডি।”
“একটা কথা ওকে একটু বলে দিন তা হলে।”
পিয়া বলতে শুরু করল, আর ফকিরকে সেটা বাংলায় বলে দিতে লাগল কানাই। ভাল করে বুঝিয়ে পিয়া বলল ওই গর্জনতলার দহে যেরকম শুশুক আসে সেইরকম শুশুক নিয়ে ও গবেষণা করছে। গত দু’দিনে ও বুঝতে পেরেছে–আর ফকির সেটা আগে থেকেই জানে–যে দিনের বেলা জল যখন বাড়তে থাকে তখন শুশুকগুলো খাবারের খোঁজে দহটা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু কোন পথ দিয়ে কীভাবে ওরা চলাফেরা করে সেটা দেখতে আর বুঝতে চায় পিয়া। আর তার জন্য, ওর মনে হয়েছে, সবচেয়ে ভাল উপায় হল ফকিরকে নিয়ে আরেকবার ওই গর্জনতলায় ফিরে যাওয়া। এবার একটা বড় নৌকো নিয়ে যাবে ওরা, সম্ভব হলে একটা মোটরবোট; তারপর ওই দহটার কাছে গিয়ে নোঙর ফেলে শুশুকদের এই দৈনিক চলাচল লক্ষ করবে পিয়া। আর সে কাজে ফকির ওকে সাহায্য করবে। এই পুরো কাজটায় দিন কয়েক লাগবে–সব মিলিয়ে চার কি পাঁচদিন, কী দেখা যায় না যায় তার ওপরে নির্ভর করবে কদিন থাকতে হয়। খরচখরচা সব পিয়াই দেবে–নৌকোর ভাড়া, খাবার-দাবারের খরচ-টরচ সব–তা ছাড়াও এর জন্য একটা থোক টাকা পাবে ফকির, আর দিন প্রতি আরও কিছু টাকা দেবে পিয়া। আর সব যদি ভালয় ভালয় মেটে তা হলে একটা বোনাসও দেবে। সব মিলিয়ে মোটমাট তিনশো আমেরিকান ডলারের মতো রোজগার করতে পারবে ফকির।
পিয়া যেমন যেমন বলছিল সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ করে যাচ্ছিল কানাই। শেষ কথাটা শুনে একটা হেঁচকি তোলার মতো আওয়াজ করে দু’হাতে মুখ ঢাকা দিল ময়না।
“টাকাটা কম বললাম?” একটু ব্যস্ত হয়ে পিয়া জিজ্ঞেস করল কানাইকে।
“কম বললেন? দেখলেন না ময়না কীরকম খুশি হয়েছে? ওদের পক্ষে একটা লটারি পাওয়ার মতো ব্যাপার এটা। আর টাকাটা সত্যি সত্যিই প্রয়োজন ওদের।”
“আর ফকির কী বলছে? ও কি একটা লঞ্চ-টঞ্চের ব্যবস্থা করতে পারবে?”
একটু চুপ করে শুনল কানাই। “ও বলছে, হ্যাঁ, এ কাজটা ও করবে। এক্ষুনি ও বেরিয়ে যাবে সব ব্যবস্থা করতে। তবে কোনও মোটরবোট এখানে নেই, ভটভটি দিয়ে কাজ চালিয়ে নিতে হবে আপনাকে।”
“সেটা কী জিনিস?”
“ডিজেলে চালানো নৌকোকে এখানে ভটভটি বলে,” কানাই বলল। “ইঞ্জিনের ভটভট আওয়াজের জন্য ওগুলোর এরকম নাম দেওয়া হয়েছে।”
“কীরকম নৌকো তাতে আমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু একটা নৌকো জোগাড় করতে পারবে তো ও?” জিজ্ঞেস করল পিয়া।
“হ্যাঁ। কাল সকালেই একটা ভটভটি ও নিয়ে আসবে, আপনি দেখেশুনে নিতে পারবেন,” জবাব দিল কানাই।
“নৌকোর মালিককে ও চেনে তো?”
“হ্যাঁ। যার ভটভটি সে ওর বাবার মতো।”
ক্যানিং থেকে লঞ্চ ভাড়া করে ফরেস্ট গার্ড আর তার আত্মীয়ের সঙ্গে কী ঝামেলা হয়েছিল মনে পড়ল পিয়ার। জিজ্ঞেস করল, “আপনার কী মনে হয়, বিশ্বস্ত লোক তো?”
“হ্যাঁ, হ্যাঁ,” বলল কানাই, “আসলে আমিও চিনি লোকটাকে। ওর নাম হল হরেন নস্কর। আমার মেসোরও অনেক কাজ করে দিত ও। নিশ্চিন্তে নিতে পারেন ওর নৌকো, আমি গ্যারান্টি দিতে পারি।”
“ঠিক আছে তা হলে।”
ফকিরের দিকে একপলক তাকিয়ে পিয়া দেখল হাসি ফুটেছে ওর মুখে। এক মুহূর্তের জন্য পিয়ার মনে হল ডাঙার গোমড়ামুখো বিরক্ত চেহারাটা সরে গিয়ে নৌকোর ওপরের স্বাভাবিক মানুষটা যেন আবার ফিরে এসেছে। আবার জলের ওপর ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনায়, না বাড়িতে যে পাষাণভার চেপে থাকে বুকের ওপর তার থেকে দূরে যাওয়ার চিন্তায় ফকিরের মেজাজ খুশ হয়ে গেল সেটা অবশ্য বুঝতে পারল না পিয়া। তবে ফকিরের কাছে যার দাম আছে সেরকম কিছু করতে পেরেছে তাতেই ও খুশি।
“এই যে, শুনুন,”কানাই কনুই দিয়ে একটু ঠেলা দিয়ে বলল পিয়াকে, “ময়না কী জিজ্ঞেস করছে আপনাকে।”
“কী জিজ্ঞেস করছে?”
“বলছে আপনার মতো এত উচ্চশিক্ষিত একজন বৈজ্ঞানিকের ওর স্বামীর মতো লোকের সাহায্য নেওয়ার কেন দরকার হয়–ও তো এক বিন্দুও লেখাপড়া জানে না।”
ভুরু কোঁচকাল পিয়া। বুঝতে পারল না; সত্যিই কি ময়না এতটাই তাচ্ছিল্য করে ওর স্বামীকে, নাকি ও আসলে বোঝাতে চাইছে ফকিরের বদলে অন্য কাউকে নিয়ে যাক পিয়া? কিন্তু অন্য কোনও লোককে তো নিয়ে যেতে চায় না পিয়া–বিশেষত সে যদি আবার ওই ফরেস্ট গার্ডের মতো লোক হয়।
পিয়া কানাইকে বলল, “আপনি প্লিজ ময়নাকে বলবেন, ওর স্বামী এখানকার নদীকে খুব ভাল চেনে। ফকিরের জ্ঞান তাই আমার মতো একজন বৈজ্ঞানিকের অনেক কাজে আসতে পারে।”
কথাটা ময়নাকে বুঝিয়ে দেওয়ার পর জবাবে ও এমন কিছু একটা তীক্ষ্ণ মন্তব্য করল যে হেসে ফেলল কানাই।
“হাসছেন কেন?” জিজ্ঞেস করল পিয়া।
“এত চালাক না মেয়েটা!” হাসতে হাসতেই বলল কানাই।
“কেন? কী বলল ও?”
“‘জ্ঞান’ আর ‘গান’ এই দুটো বাংলা শব্দ নিয়ে একটু মজা করল ও। বলল ওর স্বামীর জ্ঞানটা সত্যিই একটু বেশি থেকে গানটা আরেকটু কম থাকলে অনেক সুবিধা হত।”
.
অভ্যাস
কুসুম লুসিবাড়িতে আসায় আদৌ খুশি হয়নি নীলিমা। সেইদিন সন্ধেবেলা আমাকে বলল, “জানো, কুসুম আজকে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। ওই মরিচঝাঁপির ঝামেলায় ট্রাস্টকে জড়াতে চাইছিল। ওরা চায় ওখানে কিছু চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে ট্রাস্ট ওদের সাহায্য করুক।”
“তুমি কী বললে?”
“আমি বলে দিয়েছি আমাদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়,” খুব ঠান্ডা দৃঢ় গলায় বলল নীলিমা।
“কেন সাহায্য করতে পারবে না ওদের?” প্রতিবাদ করলাম আমি। “ওরাও তো। মানুষ–অন্য সব জায়গার লোকেদের মতো ওদেরও অসুখ-বিসুখ করে, ওষুধপত্রের দরকার হয়।”
“এটা সম্ভব নয় নির্মল,” বলল নীলিমা। “এই লোকগুলো দখলদার; ওই দ্বীপের জমি তো ওদের নয়, ওটা সরকারের সম্পত্তি। অমনি উড়ে এসে জুড়ে বসে পড়লেই হয়ে গেল? ওদের যদি ওখানে থাকতে দেওয়া হয়, লোকে তো ভাববে এই ভাটির দেশের যে-কোনও দ্বীপই এরকমভাবে ইচ্ছেমতো দখল করে নেওয়া যায়। জঙ্গলটার তা হলে কী হবে? পরিবেশের কথাটা কেউ একবার ভাববে না?”
জবাবে আমি বললাম, এই লুসিবাড়িও একসময় জঙ্গল ছিল–এই জমিও সরকারের সম্পত্তি ছিল এককালে। তা সত্ত্বেও স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটনকে তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য এখানে বসতি গড়ার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। এবং এত বছর ধরে নীলিমা বলে এসেছে উনি যা করেছেন সেটা খুবই প্রশংসাহ। তফাতটা তা হলে কী? এই উদ্বাস্তুদের স্বপ্নের মূল্য কি স্যার ড্যানিয়েলের স্বপ্নের মূল্যের চেয়ে কম? উনি ধনী সাহেব আর এরা ঘরছাড়া গরিব মানুষ বলে?
“কিন্তু নির্মল, স্যার ড্যানিয়েল যা করেছিলেন সে অনেককাল আগের কথা,” বলল নীলিমা। একবার ভাবো এখন যদি সবাই সেরকম করতে শুরু করে কী হাল হবে এই গোটা জায়গাটার। জঙ্গলের কোনও চিহ্নই থাকবে না আর।”
“দেখো নীলিমা, ওই উদ্বাস্তুরা আসার আগেও কিন্তু মরিচঝাঁপিতে জঙ্গল সেভাবে ছিল না। দ্বীপের খানিকটা অংশ তো সরকারই ব্যবহার করছিল চাষবাসের জন্য। এখন পরিবেশের নামে যা বলা হচ্ছে সব বাজে কথা। যে মানুষগুলোর আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, তাদের ওই দ্বীপটা থেকে তাড়ানোর জন্যই শুধু বলা হচ্ছে এসব।”
“তা হতে পারে, কিন্তু ট্রাস্টকে আমি এই ব্যাপারে কিছুতেই জড়াতে দিতে পারি না,” নীলিমা বলল। “আমাদের পক্ষে একটু বেশি ঝুঁকি হয়ে যাবে সেটা। হাসপাতালের রোজকার কাজ কীভাবে চলে তুমি তো জানো না, জানলে বুঝতে পারতে সরকারের সুনজরে থাকার জন্য কী করতে হয় আমাদের। নেতারা যদি একবার আমাদের পেছনে লাগে তা হলে তো হয়ে গেল। সেই ঝুঁকি আমি নিতে পারি না।”
এবার পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হল আমার কাছে। “তা হলে তুমি বলতে চাইছ যে বিষয়টার ন্যায়-অন্যায় নিয়ে তোমার কোনও বক্তব্য নেই। এই লোকগুলোকে তুমি সাহায্য করবে না, তার কারণ তুমি সরকারের সুনজরে থাকতে চাও।”
হাতদুটো মুঠো পাকিয়ে কোমরের কাছে রেখে দাঁড়াল নীলিমা। বলল, “তোমার কোনও বাস্তব ধারণা নেই নির্মল। তুমি এখনও তোমার ওই দুর্বোধ্য কবিতা আর বিপ্লবের ঝাপসা স্বপ্নের জগতেই বাস করছ। কিছু একটা সত্যি সত্যি গড়ে তোলা আর সেটার স্বপ্ন দেখা এক জিনিস নয়। কোনও জিনিস গড়ে তুলতে গেলে সবসময়েই বুঝেশুনে কিছু আপোশের রাস্তা বেছে নিতে হয়।”
নীলিমা যখন এই সুরে কথা বলে তখন সাধারণত আমি তর্কের মধ্যে আর যাই না। কিন্তু এবার ঠিক করলাম আমিও ছেড়ে কথা বলব না–”যে আপোশের রাস্তা তুমি নিয়েছ সেটা খুব বুঝেশুনে বেছে নেওয়া বলে মনে হয় না আমার।”
আরও রেগে গেল নীলিমা। বলল, “নির্মল, একটা কথা আমি তোমাকে মনে করিয়ে দিতে চাই। তোমার জন্যেই কিন্তু আমরা প্রথম লুসিবাড়িতে এসেছিলাম, কারণ রাজনীতি করতে গিয়ে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলে তুমি, আর তারপর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে। আমার তো এখানে কিছুই ছিল না বাড়ির লোকজন না, বন্ধুবান্ধব না, চাকরিও না। কিন্তু আস্তে আস্তে আমি কিছু তো একটা গড়ে তুলেছি সত্যিকারের কিছু একটা, যেটা লোকের কাজে লাগছে, সামান্য হলেও যেটা মানুষের কিছু উপকারে আসছে। আর এতগুলো বছর ধরে তুমি শুধু বসে বসে আমার কাজের বিচার করে গেছ। কিন্তু এখন তো আমার কাজের ফল চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছ–এই হাসপাতালটা। আর এটাকে বাঁচানোর জন্য আমি কী করব যদি জিজ্ঞেস করো, তা হলে বলে রাখছি শোনো, মা তার বাচ্চাদের বাঁচানোর জন্য যেমন লড়াই করে, সেইভাবে শেষ পর্যন্ত লড়ে যাব আমি। এই হাসপাতালটার ভালমন্দ, এর ভবিষ্যৎ–এটাই তো আমার সব। তার কোনও ক্ষতি আমি হতে দেব না। এতদিন ধরে তোমার কাছে আমি খুব একটা কিছু চাইনি, কিন্তু এবার চাইছি–আমার একটাই অনুরোধ, মরিচঝাঁপির ব্যাপারটার মধ্যে তুমি জড়িয়ো না। আমি জানি সরকার ওদের থাকতে দেবে না ওখানে, আর এটাও জানি যারা যারা এর মধ্যে থাকবে তাদের কাউকে ওরা রেয়াত করবে না। তুমি যদি ওই উদ্বাস্তুদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ো, তা হলে আমার সারা জীবনের কাজ দিয়ে আমাকে তার মূল্য দিতে হতে পারে। এইটা মাথায় রেখো। এইটুকুই শুধু তোমার কাছে চাইছি আমি।”
আর কিছু বলার রইল না আমার। আমার চেয়ে বেশি তো আর কেউ জানে না কী ত্যাগ স্বীকার করেছে আমার জন্য ও। বুঝতে পারলাম, মরিচঝাঁপিতে গিয়ে সেখানকার বাচ্চাদের পড়ানোর স্বপ্ন শুধু আমার এ বুড়ো বয়সের ভীমরতি, অনিবার্য অবসরকে ঠেকিয়ে রাখার একটা ব্যর্থ চেষ্টা। বিষয়টা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চেষ্টা করলাম আমি।
নতুন বছর এসে পড়ল–১৯৭৯–আর কিছুদিন পরেই হাসপাতালের জন্য চাঁদা তোলার কাজে আবার বেরিয়ে পড়ল নীলিমা। কলকাতার এক ধনী মাড়োয়ারি পরিবার একটা জেনারেটর দিতে রাজি হয়েছে; ওর এক মাসতুতো ভাই রাজ্য সরকারের মন্ত্রী হয়েছে, তার সঙ্গেও একবার দেখা করতে চায় নীলিমা। এমনকী মোরারজি দেশাই সরকারের এক বড় অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে একবার দিল্লিও যেতে হতে পারে। এত কিছু কাজ ওকে সামলাতে হবে।
নীলিমা যেদিন গেল, জেটি পর্যন্ত ওকে এগিয়ে দিতে গেলাম আমি। ঠিক নৌকোয় ওঠার মুখে ও বলল,”নির্মল, মরিচঝাঁপি নিয়ে যা বলেছি মনে রেখো। ভুলে যেয়ো না কিন্তু।”
নৌকো ছেড়ে দিল, আর আমিও ফিরে এলাম আমার পড়ার ঘরে। মাস্টারির কাজ মিটে গেছে, সময় কাটানোই এখন সমস্যা। বহু বছর পর আবার আমার খাতাটা খুললাম, ভাবলাম দেখি যদি কিছু লিখতে পারি। অনেকদিন ধরেই ভেবেছি একটা বই লিখব এই ভাটির দেশ নিয়ে–এত বছরে যা দেখেছি এখানে, যা কিছু জেনেছি জায়গাটার সম্পর্কে, সব থাকবে তাতে।
কয়েকদিন নিয়ম করে টেবিলটায় এসে বসলাম। বসে বসে দূরে রায়মঙ্গলের মোহনার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কত কথাই যে মনে এল। মনে পড়ল, যখন প্রথম এই লুসিবাড়িতে এলাম আমি, সূর্যাস্তের সময় পাখির ঝাঁকে অন্ধকার হয়ে যেত আকাশ। বহু বছর আর তত পাখি একসঙ্গে দেখি না। প্রথম যখন লক্ষ করলাম পাখির সংখ্যা কমে এসেছে, ভাবলাম হয়তো সাময়িক ব্যাপার, আবার পরে ফিরে আসবে ঝাঁকে ঝাকে। কিন্তু এল না। মনে পড়ল, একটা সময় ছিল যখন ভাটার সময় নদীর পাড়গুলো লাল হয়ে থাকত–চারদিকে থিকথিক করত লক্ষ লক্ষ কঁকড়া। সেই রং আস্তে আস্তে ফিকে হতে শুরু করল, এখন তো দেখাই যায় না আর। মনে মনে ভাবি গেল কোথায় সেই লক্ষ লক্ষ কঁকড়া? সেই পাখির ঝক?
বয়স মানুষকে মৃত্যুর চিহ্নগুলি চিনে নিতে শেখায়। হঠাৎ একদিনে সেগুলো দেখা যায় না; অনেক বছর ধরে ধীরে ধীরে বোঝা যেতে থাকে তাদের উপস্থিতি। এখন আমার মনে হল সর্বত্র সেই চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি আমি–আমার মধ্যে শুধু নয়, এই গোটা জায়গাটায়, যেখানে তিরিশটা বছর আমি কাটিয়ে দিয়েছি। পাখিরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে, মাছের সংখ্যা কমে আসছে, দিনে দিনে সমুদ্রে তলিয়ে যাচ্ছে জমি। কতটুকু লাগবে এই গোটা ভাটির দেশটা জলের তলায় চলে যেতে? বেশি নয়–সমুদ্রের জলের স্তরের সামান্য একটুখানি হেরফেরই যথেষ্ট।
এই সম্ভাবনাটা নিয়ে যত ভাবতে লাগলাম, আমার মনে হতে লাগল খুব একটা সাংঘাতিক ক্ষতি কিছু হবে না সেরকম ঘটনা ঘটলে। এত যন্ত্রণার সাক্ষী এই দ্বীপগুলো–এত কষ্ট, এত দারিদ্র্য, এত বিপর্যয়, এত স্বপ্নভঙ্গ–এগুলো যদি আজকে হারিয়েও যায়, হয়তো মানবজাতির পক্ষে অকল্যাণকর হবে না সেটা।
তারপর মরিচঝাঁপির কথা মনে পড়ল আমার–যে জায়গাকে আমার মনে হচ্ছে কেবল চোখের জলে ভেজা, সেই একই দেশ তো কারও কারও কাছে সোনার সমান। কুসুমের গল্প মনে পড়ে গেল আমার–মনে পড়ল সেই দূর বিহারে ওর নির্বাসনের দিনগুলি, কেমন তখন ওরা এই ভাটির দেশে ফেরার স্বপ্ন দেখত, এই কাদামাটি এই জোয়ার-ভাটা কেমন ওদের মনকে টানত সেই কাহিনি মনে পড়ল। আরও বাকি যারা এসেছে মরিচঝাঁপিতে, কত কষ্ট সহ্য করেছে ওরা এখানে আসার জন্য, সেই কথাও মনে এল আমার। কীভাবে এই জায়গার প্রতি সুবিচার করতে পারি আমি? এমন কী লিখতে পারি এই দেশ সম্পর্কে আমি যা ওদের মনের টান আর ওদের স্বপ্নের সমান শক্তি ধরবে? কীরকম চেহারা হবে সে লাইনগুলোর? ঠিক করে উঠতে পারলাম না। আমি–নদীর মতো বহমান হবে কি সে লেখার গতি, না ছন্দোময় হবে জোয়ার-ভাটার মতো?
বইখাতা সব সরিয়ে রাখলাম আমি, ছাদে গিয়ে জলের দিকে তাকালাম। সেই মুহূর্তে আমার চোখে প্রায় অসহ্য লাগল ওই দৃশ্য। মনে হল দুই দিক থেকে দুই প্রচণ্ড টানে বুকটা ভেঙে যাচ্ছে আমার একদিকে আমার স্ত্রী, আরেকদিকে আমার বাগদেবী সেই নারী, যেরকম কেউ আগে আমার জীবনে কখনও আসেনি; একদিকে ধীর শান্ত দৈনন্দিন পরিবর্তনের জগৎ, আরেকদিকে বিপ্লবের মাতাল করা উত্তেজনা–একদিকে গদ্য, আরেকদিকে পদ্য।
ফিরে ফিরে মনে হতে লাগল, এই দ্বিধার কথা কল্পনা করে কি মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছি। আমি? এইসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার অধিকার কি আমি কখনও অর্জন করেছি?
সেই মুহূর্তে সেই জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম আমি, যেখানে কবির কথায় আমরা নিজেদের বলি–
‘হয়তো বা বাকি থাকে কোনো
ঢালুতে দাঁড়ানো বৃক্ষ, দ্রষ্টব্য দিনের পরে দিন,
কিংবা কাল যেখানে হেঁটেছিলাম, সেই পথ,
আর কোনো জট বাঁধা অভ্যাসের অদম্য সাধুতা–
বিদায়ে যা পরাত্মখ, আমাদের ভক্ত সহবাসী।’
.
একটি সূর্যাস্ত
বিকেল ফুরিয়ে এসেছে। সূর্য ঢলে পড়েছে বিদ্যার মোহনায়। পিয়া ঠিক করল কানাইয়ের আমন্ত্রণের সুযোগটা নেবে একবার গেস্ট হাউসের ছাদে উঠে পড়ার ঘরের দরজায় গিয়ে কড়া নাড়ল ও।
“কে?” চোখ পিটপিট করতে করতে এসে দরজাটা খুলল কানাই। মনে হল একটা ঘোর থেকে যেন জেগে উঠেছে।
“ডিস্টার্ব করলাম?”
“না না, সেরকম কিছু না।”
“ভাবলাম একটু সূর্যাস্ত দেখি ছাদ থেকে।”
“গুড আইডিয়া–ভালই করেছেন চলে এসে।” হাতের বাঁধানো খাতাটা রেখে দিয়ে, পিয়ার সঙ্গে ছাদের পাঁচিলের ধারে এসে দাঁড়াল কানাই। শেষ বেলার সূর্যের আলোয় দূরে আকাশ আর মোহনায় তখন আগুন লেগেছে।
“অসাধারণ, তাই না?” জিজ্ঞেস করল কানাই।
“সত্যিই অসাধারণ।”
লুসিবাড়ির দ্রষ্টব্যগুলি এক এক করে পিয়াকে দেখাতে লাগল কানাই–ময়দান, হ্যামিলটনের কুঠি, হাসপাতাল, আরও এটা ওটা। দেখানো যখন শেষ হল ততক্ষণে ঘুরে ছাদের উলটোদিকটায় চলে এসেছে ওরা–সকালে যে রাস্তা ধরে গিয়েছিল, সেটার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। হাসপাতালের স্টাফ কোয়ার্টার্সগুলি সামনে চোখে পড়ছে। পিয়া বুঝতে পারল দু’জনেই ওরা ফকিরের বাড়ির ঘটনার কথা ভাবছে।
“কাজগুলো যে সব ঠিকঠাক হয়েছে আজকে, ভেবেই বেশ ভাল লাগছে আমার,” পিয়া বলল।
“সব ঠিকঠাক হয়েছে মনে হয় আপনার?”
“হ্যাঁ, মনে হয়,” বলল পিয়া। “অন্তত ফকির তো আবার যেতে রাজি হয়েছে। শুরুতে আমার বেশ সন্দেহই ছিল ও যাবে কিনা।”
“সত্যি কথা বলতে কী, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কী ভাবা উচিত,” কানাই বলল। “এমন অদ্ভুত গোমড়া টাইপের ছেলে, কখন কী করবে বোঝা কঠিন।”
“কিন্তু বিশ্বাস করুন, যখন নৌকোয় থাকে তখন ও একেবারে অন্য মানুষ।”
“আপনি ঠিক জানেন, আপনার কোনও অসুবিধা হবে না ওর সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে?”
জিজ্ঞেস করল কানাই। “বেশ কয়েকটা দিনের মামলা কিন্তু।”
“হ্যাঁ, জানি।” পিয়া বুঝতে পারছিল ফকিরের বিষয়ে কানাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে গেলেই অদ্ভুত একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। বিশেষত সকালের সেই নীরব ভর্ৎসনার ব্যাপারটা এখনও ভুলতে পারেনি কানাই। পিয়া আস্তে আস্তে বলল, “আমাকে ফকিরের মায়ের কথা বলুন না। কেমন মানুষ ছিলেন উনি?”
একটু ভাবল কানাই। “ফকির একদম ওর মায়ের চেহারাটা পেয়েছে,” বলল অবশেষে। “কিন্তু আর কোনও মিল খুঁজে পাওয়া মুশকিল। কুসুম ছিল টগবগে স্বভাবের মেয়ে, সবসময় হাসত, মজা করত। ফকিরের মতো একটুও নয়।”
“কী হয়েছিল ওনার?”
“সে অনেক লম্বা গল্প,” জবাব দিল কানাই। “সবটা আমি জানিও না। এটুকু শুধু বলতে পারি, পুলিশের সঙ্গে একটা গণ্ডগোলে মারা গিয়েছিল ও।”
ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেল পিয়া। “কী করে?”
“একদল রিফিউজি এখানকার একটা দ্বীপ দখল করে বসেছিল–ও-ও তাদের সঙ্গে ছিল। কিন্তু সে জমির মালিকানা ছিল সরকারের। ফলে গোলমাল বাধল, আর বহু লোক মারা গেল। ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯৭৯ সালে ফকিরের বয়স তখন খুব বেশি হলে পাঁচ কি ছয়। ওর মা মারা যাওয়ার পরে হরেন নস্কর ওকে এনে মানুষ করে। হরেনই ওর বাবার মতো।”
“মানে ফকিরের জন্ম এখানে নয়?”
“না। ওর জন্ম হয়েছিল বিহারে,” বলল কানাই। “ওর বাবা-মা ওখানে থাকত তখন। তারপর ওর বাবা মারা যাওয়ার পর ওর মা ওকে নিয়ে এখানে চলে আসে।”
পিয়ার মনে পড়ল কল্পনায় ফকিরের পরিবারের কীরকম ছবি দেখেছিল ও–কীরকম দেখেছিল ওর বাবা-মা-র চেহারা, অনেক ভাইবোন। নিজের অন্তদৃষ্টির অভাবে নিজেরই খুব লজ্জা লাগল ওর। “এই একটা ব্যাপারে তা হলে ফকির আর আমার একটু মিল আছে,” বলল পিয়া।
“কী ব্যাপারে।”
“মাকে ছাড়া বড় হয়ে ওঠা।”
“আপনারও কি ছোটবেলায় মা মারা গিয়েছিলেন?” জিজ্ঞেস করল কানাই।
“ওর মতো অতটা ছোট ছিলাম না। আমার বারো বছর বয়সে মারা যান, আমার মা। ক্যানসার হয়েছিল। আমার অবশ্য মনে হয় তার অনেক আগে থেকেই মাকে হারিয়েছিলাম আমি,” পিয়া বলল।
“কেন?”
“কারণ আমাদের থেকে–মানে আমার বাবা আর আমার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিল মা। ডিপ্রেশনে ভুগত। আর যত দিন গেছে অসুখটা বাড়তেই থেকেছে।”
“আপনার নিশ্চয়ই খুব কষ্টে কেটেছে সেই সময়টা?”
“মায়ের থেকে বেশি নয়,” পিয়া বলল। “মা কেমন ছিল জানেন, খানিকটা যেন অর্কিডের মতো, দুর্বল অথচ সুন্দর, অনেক অনেক লোকের যত্ন আর ভালবাসার ওপর নির্ভরশীল। মা যে ধরনের মানুষ ছিল, তাতে বাড়ি থেকে এতটা দূরে না গেলেই পারত। আমেরিকায় তো মা-র কিছুই ছিল না–বন্ধুবান্ধব না, কাজের লোকজন না, চাকরি না, নিজস্ব কোনও জীবনই ছিল না। ওদিকে বাবা ছিল যাকে বলে এক্কেবারে খাঁটি প্রবাসী–উদ্যমী, পরিশ্রমী, সফল মানুষ। নিজের কেরিয়ার নিয়েই ব্যস্ত সবসময়। আর আমি ব্যস্ত আমার স্বাভাবিক ছেলেমানুষি খেলাধুলো পড়াশোনা নিয়ে। আমার মনে হয় একটা হতাশার মধ্যে আস্তে আস্তে তলিয়ে যেতে শুরু করেছিল মা। তারপর একটা সময় এসে নিজেই হাল ছেড়ে দিয়েছিল।”
ওর হাতের ওপর হাত রেখে একটু চাপ দিল কানাই। “খুব খারাপ লাগছে আমার।”
কানাইয়ের কথার সুরের মধ্যে এমন কিছু একটা ছিল যেটা খুব অবাক করল পিয়াকে। ওকে সবসময় মনে হয়েছে ভীষণ আত্মকেন্দ্রিক, অন্যদের ব্যাপার নিয়ে কখনওই মাথা ঘামায় না। কিন্তু এখন ওর গলায় যে সহানুভূতির সুর সেটা তো আন্তরিক বলেই মনে হল।
একটু হেসে পিয়া বলল, “ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। আপনি বলছেন আমার জন্য আপনার খারাপ লাগছে, কিন্তু ফকিরের জন্য তো আপনার বিশেষ সহানুভূতি আছে বলে মনে হচ্ছে না। অথচ আপনি ওর মাকে চিনতেন। কেন বলুন তো?”
কথাটা শুনে শক্ত হয়ে গেল কানাইয়ের চোয়াল, তারপর একটু বাঁকা সুরে হেসে উঠল ও। বলল, “ফকিরের কথা যদি বলেন, তা হলে আমি বলব আমার সহানুভূতি ওর বউয়ের জন্যই বেশি।”
“তার মানে?”
“আজ সকালে ময়নার জন্য একটুও খারাপ লাগেনি আপনার?” জিজ্ঞেস করল কানাই। “একবার ভাবুন তো, ওরকম একটা লোকের সঙ্গে জীবন কাটানো কীরকম কঠিন ব্যাপার। তার ওপরে রুটিরুজি বলুন, মাথার ওপরে একটা ছাদ বলুন, সেসব কথাও তো ওকেই ভাবতে হয়। কী অবস্থা থেকে ও উঠে এসেছে কল্পনা করুন একবার ওর জাতপাতের সমস্যা, ওর বাড়ির পরিবেশ তার মধ্যে থেকেও যে আজকের দুনিয়ায় বেঁচে থাকার জন্য কী করা দরকার সেটা মাথা খাঁটিয়ে বের করেছে ও, সেই ব্যাপারটা প্রশংসাজনক নয়? আর শুধু যেনতেনভাবে বেঁচে থাকা নয়, ভালভাবে বাঁচতে চায় ও, নিজেকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।”
মাথা নাড়ল পিয়া। “বুঝেছি।” এতক্ষণে ও উপলব্ধি করল, কানাইয়ের পক্ষে এই লুসিবাড়ির মতো জায়গায় এসে ময়নার মতো একজন মেয়ের দেখা পাওয়াটা খুবই ভরসার কথা–নিজের জীবনে যে পথ কানাই বেছে নিয়েছে, ময়নার গোটা অস্তিত্বটা ওর কাছে যেন সেই পথেরই যৌক্তিকতা প্রমাণ করছে। কানাইয়ের পক্ষে বিশ্বাস করা খুবই জরুরি যে ওর নিজস্ব মূল্যবোধগুলো আসলে সমদর্শী, সংস্কারমুক্ত, গুণবাদী। ও মনে মনে ভাবতে পারলে ভরসা পাবে যে, “আমি নিজের জন্য যা চাই অন্য সকলের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে তার আসলে কোনও তফাত নেই। বড়লোক গরিবলোক নির্বিশেষে যে কারওই সামান্য একটু উদ্যম আছে, একটু ক্ষমতা আছে, সে-ই চায় এই পৃথিবীতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে–ময়নাই তার জ্বলন্ত প্রমাণ।” পিয়া বুঝতে পারল, যে আয়নায় কানাই নিজেকে দেখছে, ফকিরের মতো মানুষ সেখানে গাড়ির রিয়ারভিউ মিররের ওপর একটা ছায়া ছাড়া কিছু নয়, দ্রুত মিলিয়ে যাওয়া একটা উপস্থিতি মাত্র, চির-অতীত লুসিবাড়ি থেকে উঠে আসা ভূতের মতো। কিন্তু এটাও আন্দাজ করতে পারে পিয়া যে কানাই যে দেশে বাস করছে, সমস্ত নতুনত্ব এবং কর্মচাঞ্চল্য সত্ত্বেও এরকম অসংখ্য অদেখা ছায়াশরীরের উপস্থিতি সেখানে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না, যত জোরেই চিৎকার করা যাক না কেন, তাদের ফিসফিসে কণ্ঠস্বর পুরোপুরি চাপা দেওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।
“আপনি সত্যিই ময়নাকে পছন্দ করেন, তাই না?” পিয়া জিজ্ঞেস করল।
“ঠিক কথাটা যদি জানতে চান, তা হলে বলব ওকে শ্রদ্ধা করি আমি,” জবাব দিল কানাই।
“সেটা আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু ফকিরের জায়গা থেকে যদি দেখেন, তা হলে ওর চেহারাটা হয়তো একটু অন্যরকম দেখাবে।”
“কী বলতে চাইছেন আপনি?”
“নিজেকে জিজ্ঞেস করেই দেখুন না,” বলল পিয়া। “ও যদি আপনার স্ত্রী হত তা হলে কেমন লাগত আপনার?”
হো হো করে হেসে উঠল কানাই। তারপর আবার যখন কথা বলতে শুরু করল তখন ওর গলার সুরের চটুলতায় দাঁতে দাঁত ঘষল পিয়া। “ময়না যে ধরনের মেয়ে তাতে ওর সঙ্গে ছোটখাটো একটা এক্সাইটিং সম্পর্কের কথা ভাবা চলতে পারে,” বলল কানাই। “মানে যাকে আমরা বলতাম ফ্লিং। কিন্তু তার থেকে বেশি কিছু নয়। সেরকম ক্ষেত্রে আপনার মতো কোনও মহিলাই আমার বেশি পছন্দের।”
হাতটা তুলে কানের দুলে আস্তে আস্তে আঙুল বোলাল পিয়া, খানিকটা যেন ভরসা পাওয়ার জন্য। তারপর একটু সতর্ক হাসি হেসে বলল, “আপনি কি ফ্লার্ট করছেন আমার
সঙ্গে, কানাই?”
“কী মনে হয়?” একগাল হেসে কানাই পালটা প্রশ্ন করল।
“আমার অভ্যেস চলে গেছে,” বলল পিয়া।
“তা হলে তো সে ব্যাপারে কিছু করা উচিত আমাদের, তাই না?”
নীচের থেকে ভেসে আসা একটা চিৎকারে কথা থেমে গেল ওর। “কানাইবাবু!”
পাঁচিলের ওপর থেকে ঝুঁকে ওরা দেখল নীচের রাস্তার ওপর ফকির দাঁড়িয়ে রয়েছে। পিয়াকে দেখতে পেয়ে চোখ নামাল ও, মাটিতে পা ঘষতে লাগল আস্তে আস্তে। তারপর কানাইয়ের উদ্দেশ্যে দু’-একটা কী কথা বলেই হঠাৎ ঘুরে বাঁধের দিকে হেঁটে চলে গেল।
“কী বলল ও?” জিজ্ঞেস করল পিয়া।
“আপনাকে জানিয়ে দিতে বলল যে হরেন নস্কর কালকে ওর ভটভটি নিয়ে এখানে আসবে। আপনি গিয়ে দেখে নিতে পারেন। আর যদি মনে হয় ওটায় কাজ হবে, তা হলে পরশু সকালে রওয়ানা হয়ে যেতে পারেন, কানাই বলল।
“চমৎকার,” বলে উঠল পিয়া। “আমি বরং গিয়ে আমার জিনিসপত্রগুলি গুছিয়ে গাছিয়ে নিই।”
পিয়া লক্ষ করল মাঝপথে বাধা পড়ায় ও নিজে যতটা খুশি হয়েছে, ঠিক ততটাই বিরক্ত হয়েছে কানাই। ভুরুটা একটু কুঁচকে ও বলল, “আমারও মনে হয় এবার গিয়ে মেসোর খাতাটা নিয়ে বসা উচিত।”
.
রূপান্তর
হরেন যদি না থাকত, আবার হয়তো আমি আমার পুরনো অভ্যাসের চক্রেই ফিরে যেতাম; প্রবল ভালবাসায় যে অভ্যাসগুলো আঁকড়ে ধরে থাকে আমাকে, ছেড়ে যেতে চায় না কিছুতেই, তাদের মধ্যে থেকেই হয়তো সুখে কাটিয়ে দিতাম বাকি দিনগুলি। কিন্তু একদিন ঠিক খুঁজতে খুঁজতে এসে উপস্থিত হল হরেন। বলল, “সার, পৌষমাস তো শেষ হয়ে এল। বনবিবির পুজো তো এসেই গেল প্রায়। কুসুম আর ফকির একদিন গর্জনতলা যাবে বলছিল, তো আমি বলেছি ওদের নিয়ে যাব। কুসুম বলল আপনাকে একবার জিজ্ঞেস করতে, যদি যান।”
“গর্জনতলা? সেটা আবার কোথায়?”
“জঙ্গলের অনেক ভেতরে। ছোট একটা দ্বীপ। কুসুমের বাবা সেখানে বনবিবির একটা মন্দির বানিয়েছিল, তাই ও একবার যেতে চায় ওখানে।”
এ আরেক নতুন সমস্যা। এর আগে সব সময়ই যে-কোনও ধর্মীয় ব্যাপার থেকে আমি সাবধানে দূরে সরে থেকেছি। তা যে শুধু ধর্ম বিশ্বাসকে ভ্রান্ত চেতনা বলে মনে করি সে জন্যই নয়, সেই বিশ্বাস কত ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে দেশ বিভাগের সময় সেটা নিজের চোখে দেখেছি বলেও বটে। আর হেডমাস্টার হিসেবেও আমার মনে হয়েছে, হিন্দুই বল বা মুসলমানই বল, কোনও ধর্মের সঙ্গেই না জড়ানোটা আমার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। একটু আশ্চর্যের মনে হলেও, সেই কারণেই কখনও বনবিবির পুজো দেখিনি আমি, আর এই দেবীটি সম্পর্কে কোনও আগ্রহও কখনও হয়নি আমার। কিন্তু এখন তো আমি আর হেডমাস্টার নেই, কাজেই সেই নিয়মটাও আর খাটে না।
কিন্তু নীলিমা যে বারণ করে গেল, তার কী হবে? ও যে বার বার করে আমাকে মরিচঝাঁপি থেকে দূরে সরে থাকতে অনুরোধ করে গেল? নিজেকে বোঝালাম, এর সঙ্গে তো সেভাবে দেখতে গেলে মরিচঝাঁপির কোনও সম্পর্ক নেই, কারণ আমরা তো যাচ্ছি অন্য একটা দ্বীপে। “ঠিক আছে হরেন, আমি যাব গর্জনতলা। কিন্তু মনে রেখো, মাসিমার কানে যেন একটা কথাও না যায়।”
“সে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন সার।”
পরদিন ভোরবেলা হরেন এল, আর আমরা বেরিয়ে পড়লাম।
শেষ যেবার মরিচঝাঁপি এসেছিলাম তারপর কয়েকমাস কেটে গেছে। সেখানে পৌঁছতেই চোখে পড়ল অনেক পরিবর্তন হয়েছে এর মধ্যে : আগের সেই উদ্দীপনা কেটে গেছে, একটা ভীতি আর সন্দেহর পরিবেশ যেন চেপে ধরেছে দ্বীপটাকে। একটা কাঠের ওয়াচ টাওয়ার বানানো হয়েছে, উদ্বাস্তুরা ছোট ছোট দলে নদীর পাড় ধরে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছে। নৌকো পাড়ে ভিড়তেই বেশ কয়েকজন লোক এসে ঘিরে ধরল আমাদের। তারপর নানা জেরা। আপনাদের পরিচয় কী? কী দরকারে এসেছেন এখানে?
একটু অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যেই গিয়ে পৌঁছলাম কুসুমের কুঁড়েতে। দেখলাম ও-ও একটু মানসিক চাপের মধ্যে রয়েছে। বলল কয়েক সপ্তাহ ধরেই নানাভাবে আরও চাপ দিতে শুরু করেছে সরকার। কয়েক জন অফিসার, পুলিশের লোকজন ঘুরে গেছে এর মধ্যে। দ্বীপ ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য উদ্বাস্তুদের প্রথমে নানা রকম লোভ দেখিয়েছে। তাতে কাজ না হওয়ায় তারপর সরাসরি হুমকি দিয়েছে। যদিও হটেনি উদ্বাস্তুরা, কিন্তু একটা ভীতির পরিবেশ তৈরি হয়েছে : কেউ জানে না কী হবে এবার।
বেলা হয়ে গিয়েছিল, তাই পা চালিয়ে চললাম আমরা। কুসুম আর ফকির বনবিবি এবং তার ভাই শা জঙ্গলির ছোট ছোট মূর্তি গড়ে এনেছিল মাটি দিয়ে, সেগুলিকে হরেনের নৌকোয় তোলা হল। তারপর দ্বীপ ছেড়ে রওয়ানা হলাম আমরা।
নদীতে বেরিয়ে পড়বার পর স্রোতের টানে সবার মেজাজ ভাল হয়ে গেল। চারপাশে আরও অনেক নৌকো দেখতে পেলাম, সবাই কোথাও না কোথাও যাচ্ছে। পুজো দিতে। কয়েকটা নৌকোয় দেখলাম কুড়ি-ত্রিশজন পর্যন্ত লোক আছে। সুন্দর রং করা বনবিবি আর শা জঙ্গলির বিশাল বিশাল মূর্তি নিয়ে যাচ্ছে তারা, সঙ্গে গানের লোকজন আর ঢাকঢোলও আছে দেখলাম।
আমাদের নৌকোয় শুধু আমরা চারজন–হরেন, ফকির, কুসুম আর আমি।
“তোমার ছেলেমেয়েদের নিয়ে এলে না কেন হরেন? তারা সব কোথায়?” জিজ্ঞেস করলাম আমি।
“ওরা সব আমার শ্বশুরবাড়ির লোকেদের সঙ্গে গেছে,” কেমন একটু মিনমিন করে জবাব দিল হরেন। “ওদের নৌকোটা বড়।”
একটা মোহনায় এসে পৌঁছলাম আমরা। মোহনা পেরোতে পেরোতে লক্ষ করলাম কোনও মন্দির অথবা ঠাকুর দেবতার মূর্তি-টুর্তির সামনে এলে মানুষ যেমন করে, হরেন আর কুসুম সেই রকম ভক্তিভরে বারবার নমস্কার করছে। ফকির দেখলাম খুব মন দিয়ে লক্ষ করছে, আর ওদের দেখাদেখি ও-ও হাতদুটো একবার কপালে ঠেকাচ্ছে, আরেকবার বুকের কাছে নিয়ে আসছে।
“কী ব্যাপার বল তো?” একটু আশ্চর্য হয়েই জিজ্ঞেস করলাম আমি। “কী দেখতে পেলে তোমরা? এখানে তো কোনও মন্দির-টন্দির নেই? আমি তো চারিদিকে জল ছাড়া আর কিছু দেখছি না।”
হেসে উঠল কুসুম। প্রথমে তো কিছুতেই বলবে না, তারপর একটু সাধাসাধি করতে শেষে বলল, ভাটির দেশকে ভাগ করার জন্য বনবিবি যে গণ্ডী টেনে দিয়েছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে, ওই মাঝ-মোহনায় আমরা সেই গণ্ডী পেরোলাম। অর্থাৎ মানুষদের জগৎ আর দক্ষিণরায় এবং তার চেলা চামুণ্ডা সব দৈত্য দানবদের জগতের মাঝের সীমানাটা পেরিয়ে এলাম আমরা। ভেবে একটু শিউরে উঠলাম যে আমার কাছে একটা সত্যিকারের কাটাতারের বেড়া যেরকম, কুসুম আর হরেনের কাছে এই কাল্পনিক রেখা ঠিক সেরকমই বাস্তব।
আমার চোখেও এখন যেন চারিদিকের দৃশ্য সব নতুন ঠেকতে লাগল–সবকিছুই মনে হতে লাগল অপ্রত্যাশিত, বিস্ময়কর। সময় কাটানোর জন্য একটা বই নিয়েছিলাম সঙ্গে, কিন্তু এখন মনে হল একদিক থেকে দেখতে গেলে তো এই ভূদৃশ্যের সঙ্গে বইয়ের খুব একটা তফাত নেই–এও তো ঠিক সেই পর পর সাজানো পাতার মতো, কিন্তু একটা পাতা আরেকটার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই বই মানুষ খোলে নিজের নিজের রুচি এবং শিক্ষা, স্মৃতি এবং সাধ অনুযায়ী : একজন ভূতাত্ত্বিকের চোখের সামনে তার এক রকম পাতা খুলে যায়, নৌকোর মাঝি দেখতে পায় অন্য এক পাতা, জাহাজের পথপ্রদর্শক বা শিল্পীর জন্যেও সে রকম আলাদা আলাদা পাতা রয়েছে এ বইয়ে। কখনও কখনও সে পাতার লাইনগুলির নীচে দাগ টানা থাকে, যে দাগ কিছু মানুষ দেখতেই পায় না, আবার কিছু মানুষের কাছে সে দাগ প্রত্যক্ষ বাস্তব, বৈদ্যুতিক তারের মতোই মারাত্মক।
আমার মতো একজন শহুরে লোকের কাছে এই ভাটির দেশের জঙ্গল ছিল শুধুমাত্র এক শূন্যতা, যেখানে সময় স্থির হয়ে আছে। এখন আমি বুঝতে পারলাম, সে ছিল আমার চোখের ভুল। আসল ঘটনা ঠিক তার উলটো। সময়ের চাকা এখানে এত দ্রুত ঘুরছে যে তা চোখে দেখাই যায় না। অন্য জায়গায় একটা নদীর গতিপথ বদলাতে কয়েক দশক লাগে, কখনও কখনও কয়েকশো বছর পর্যন্ত লেগে যায়; এক যুগ লেগে যায় একটা দ্বীপ গড়ে উঠতে। কিন্তু পরিবর্তনই হল ভাটির দেশের ধর্ম। এক এক সপ্তাহে এখানে নদীর খাত বদলায়, দিনে দিনে গড়ে ওঠে বা মিলিয়ে যায় গোটা দ্বীপ। অন্য জায়গায় নতুন করে একটা জঙ্গল তৈরি হতে কয়েক শতক, এমনকী কয়েক হাজার বছর পর্যন্ত লেগে যায়, কিন্তু এখানে মাত্র দশ কি পনেরো বছরে নেড়া একটা দ্বীপ ঢেকে যায় ঘন বাদাবনে। এরকম কি হতে পারে, যে পৃথিবীর ছন্দটাই অনেক দ্রুত হয়ে গেছে এখানে এসে? আর সেইজন্যই এত তাড়াতাড়ি এখানে ঘটছে সমস্ত কিছু?
রয়্যাল জেমস অ্যান্ড মেরি নামের সেই বিলিতি জাহাজের কথা মনে পড়ে গেল আমার। ১৬৯৪ সালে সেই জাহাজ এই ভাটির দেশের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। রাতের অন্ধকারে এক চড়ায় ধাক্কা খেয়ে বহু মাস্তুলবিশিষ্ট সেই বিশাল সমুদ্রপোত তলিয়ে গেল জলে। ক্যারিবিয়ান সাগর কি ভূমধ্যসাগরের শান্ত জলে যদি এই দুর্ঘটনা ঘটত, তা হলে কী হত? সাগরতলের প্রাণী এবং উদ্ভিদে নিশ্চয়ই ছেয়ে যেত সে ধ্বংসাবশেষ এবং সেই অবস্থাতেই রয়ে যেত শত শত বছর। ডুবুরি আর অভিযাত্রীরা নিশ্চয়ই সেখানে নেমে খুঁজে বেড়াত হারিয়ে যাওয়া ধনরত্ন। কিন্তু এখানে? মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে সেই বিশাল জাহাজটাকে স্রেফ হজম করে ফেলল এই ভাটির দেশ। এতটুকু চিহ্নও আর রইল না কোথাও।
.
এটাই এরকম একমাত্র ঘটনা নয়। স্মৃতির পথে পিছু হাঁটতে হাঁটতে মনে পড়ল এমন অসংখ্য প্রাচীন জাহাজের সলিল সমাধি ঘটেছে এই ভাটির দেশের নদী-খাঁড়িতে। সেই ১৭৩৭-এর ভয়ংকর ঝড়ে তো দু’ডজনেরও বেশি জাহাজডুবি হয়েছিল এখানে। আর ১৮৮৫-তে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্টিম নেভিগেশন কোম্পানির গর্ব সেই দুই স্টিমার, আর্কট আর মাহরাট্টা তো এখানেই তলিয়ে গিয়েছিল জলে। আর ১৮৯৭-এ সিটি অব ক্যান্টারবেরির ডুবে যাওয়ার ঘটনাই বা ভুলি কী করে? কিন্তু সেসব দুর্ঘটনার জায়গায় গেলে কিছুই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না এখন। এই হিংস্র স্রোতের করাল গ্রাস থেকে কোনও কিছুরই কোনও ছাড় নেই; সব কিছুই গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে শেষ পর্যন্ত মিহি পলির চেহারা নেয়, রূপান্তর ঘটে পরিণত হয় নতুন কোনও পদার্থে।
মনে হল যেন গোটা ভাটির দেশটাই কবির কণ্ঠে বলছে : “জীবন যাপিত হয় রূপান্তরে।”
.
মরিচঝাঁপিতে এখন বিকেল। দ্বীপের এই ওয়ার্ডের উদ্বাস্তুদের মিটিং থেকে এক্ষুনি ফিরল কুসুম আর হরেন। গুজব যা শোনা গিয়েছিল সেটা সত্যি। নদীর অন্য পারে যে গুণ্ডাবাহিনী জড়ো হয়েছে ওদেরই এখানে নিয়ে আসা হবে উদ্বাস্তুদের তাড়ানোর জন্য। কিন্তু সে আক্রমণ শোনা গেল খুব সম্ভবত কাল শুরু হবে। আরও কয়েক ঘণ্টা সময় হাতে আছে আমার।