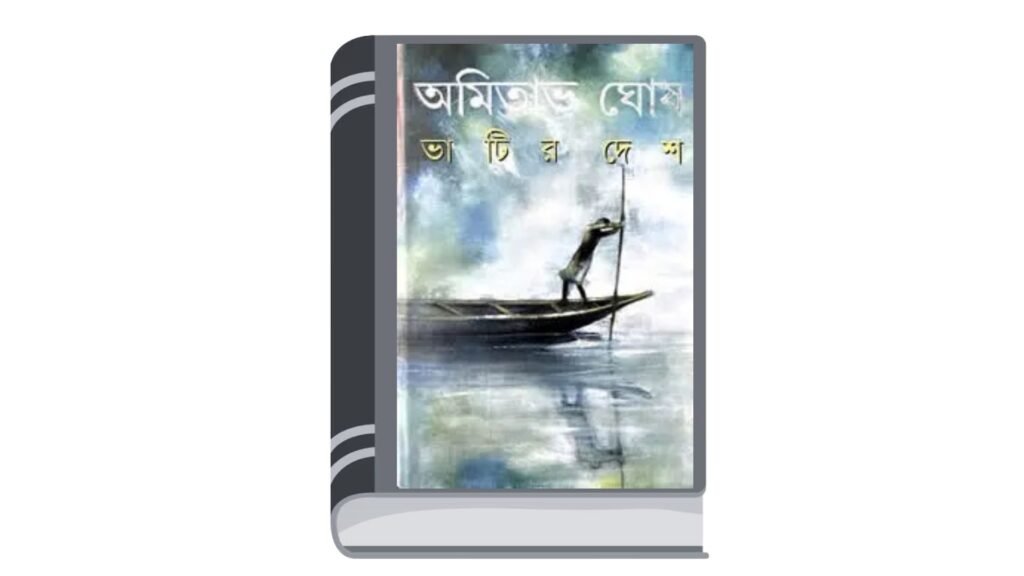২.২ দ্বিতীয় পর্ব – জোয়ার
তীর্থদর্শন
রাতের খাবার দেখে পিয়ার মনে হল ওর খাওয়া-দাওয়ার অভ্যাস সম্পর্কে ময়নাকে কেউ কিছু বলেছে। সাধারণ ভাত আর মাছের ঝোল ছাড়াও এ বেলা ময়না নিয়ে এসেছে খানিকটা আলুসেদ্ধ আর দুটো কলা। ভাল লাগল পিয়ার। হাত জোড় করে ময়নাকে ধন্যবাদ জানাল ও।
ময়না চলে যাওয়ার পর পিয়া কানাইকে জিজ্ঞেস করল ও কি এ ব্যাপারে ময়নাকে কিছু বলেছে? মাথা নাড়ল কানাই : “না তো।”
“তা হলে নিশ্চয়ই ফকির।” সাগ্রহে আরও এক হাতা আলুসেদ্ধ তুলে নিল পিয়া। “এখন শুধু একটু ওভালটিন থাকলেই সোনায় সোহাগা হত।”
“ওভালটিন?” আশ্চর্য হয়ে প্লেট থেকে চোখ তুলে তাকাল কানাই। “আপনি ওভালটিন ভালবাসেন?” মাথা নেড়ে পিয়া হ্যাঁ বলাতে হাসতে শুরু করল ও। “মার্কিন দেশেও আজকাল লোকে ওভালটিন খাচ্ছে নাকি?”
“এই অভ্যাসটা আসলে দেশ থেকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল আমার বাবা মা,” জবাব দিল পিয়া। “স্টক ফুরোলে ওখানকার ইন্ডিয়ান দোকান থেকে কিনে নিত। আর আমি পছন্দ করি কারণ জিনিসটা সঙ্গে রাখাও সহজ, আর জলে জলে ঘোরার সময় বানিয়ে খেয়ে নিতেও কোনও ঝামেলা নেই।”
“তার মানে আপনার ওই ডলফিনদের পিছু পিছু ঘুরে বেড়াবার সময় আপনি ওভালটিন খেয়েই কাটান?”
“কখনও কখনও।”
প্লেট ভরে ভাত ডাল আর হেঁচকি তুলে নিতে নিতে দুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়াল কানাই। “এই প্রাণীগুলোর জন্যে অনেক কষ্ট করেন আপনি, না?”
“আমি ঠিক সেভাবে দেখি না ব্যাপারটাকে।”
“আপনার এই জন্তুগুলো কি খুব ইন্টারেস্টিং?” জিজ্ঞেস করল কানাই। “মানে, ওদের নিয়ে চর্চা করার জন্যে আগ্রহ হতে পারে লোকের?”
“আমি তো যথেষ্টই ইন্টারেস্ট পাই,” পিয়া বলল। “আর অন্তত একটা কারণ আমি বলতে পারি যাতে আপনার মনেও একটু আগ্রহ জাগতে পারে।”
“বলুন, শুনছি,” জবাব দিল কানাই। “সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছি প্ররোচিত হইবার জন্য। বলুন, কী সেই কারণ?”
“একেবারে প্রথম দিকে যে জায়গাগুলোতে এই জাতীয় শুশুকের নমুনা পাওয়া গিয়েছিল, সেগুলির মধ্যে একটা হল কলকাতা,” পিয়া বলল। “একটু ইন্টারেস্ট পাচ্ছেন কি এবার?”
“কলকাতা?” কানাইয়ের চোখে অবিশ্বাস। “মানে আপনি বলতে চান কলকাতায় এক সময় ডলফিন দেখা যেত?”
“যেত। শুধু ডলফিন কেন, তিমি মাছও দেখা যেত এক সময়,” পিয়া বলল। “তিমি মাছ?” হেসে ফেলল কানাই। “রসিকতা করছেন?”
“রসিকতা নয়, সত্যি সত্যিই একটা সময় এইসব জলচর প্রাণীদের প্রচুর সংখ্যায় দেখতে পাওয়া যেত কলকাতায়।”
“বিশ্বাস হচ্ছে না,” স্পষ্ট জবাব কানাইয়ের। “মানে, এরকম কিছু হলে সেটা আমি নিশ্চয়ই জানতে পারতাম।”
“কিন্তু ঘটনাটা সত্যি,” বলল পিয়া। “আপনাকে বলেই ফেলি, এই যে গত সপ্তাহে আমি কলকাতা হয়ে এলাম, সেটা ছিল বলতে পারেন আমার প্রাণীবৈজ্ঞানিক তীর্থযাত্রা।”
হাসিতে ফেটে পড়ল কানাই। “প্রাণীবৈজ্ঞানিক তীর্থযাত্রা?”
“আজ্ঞে হ্যাঁ,” পিয়া বলল। “কলকাতায় আমার মাসতুতো বোনেরাও হেসেছিল কথাটা শুনে, কিন্তু সত্যি জানেন, এক বর্ণও বাড়িয়ে বলছি না, এবার কলকাতায় তীর্থেই এসেছিলাম আমি।”
“আপনার মাসতুতো বোনেরা?” জিজ্ঞেস করল কানাই।
“হ্যাঁ। আমার মাসিমার দুই মেয়ে। দু’জনেই আমার চেয়ে বয়সে ছোট। একজন স্কুলে পড়ে, আরেক জন কলেজে। বেশ ব্রাইট, স্মার্ট দুটো মেয়ে। ওরা বলল কলকাতায় যেখানে যেখানে আমি যেতে চাই, বাড়ির গাড়িতে করে নিয়ে যাবে আমায়। ড্রাইভার আছে, কোনও অসুবিধা হবে না। ওরা মনে হয় ভেবেছিল আমি টুকটাক কেনাকাটা করতে চাইব। তাই যখন বললাম আমি কোথায় যেতে চাই ওরা অবাক হয়ে গেল : বটানিকাল গার্ডেনস! ওখানে কী করতে যাবে?”
“ঠিক প্রশ্ন। বটানিকাল গার্ডেনের সঙ্গে ডলফিনের কী সম্পর্ক?” কানাই প্রশ্ন করল।
“সম্পর্ক আছে,” বলল পিয়া। “নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরিতে এই বটানিকাল গার্ডেনের ভার ছিল খুব দক্ষ কয়েকজন প্রকৃতিবিদের ওপর। তাদেরই একজন ছিলেন এই গ্যাঞ্জেটিক ডলফিনের আবিষ্কর্তা উইলিয়াম রক্সবার্গ।
“কলকাতার এই বটানিকাল গার্ডেনে বসেই ১৮০১ সালে রক্সবার্গ সেই বিখ্যাত প্রবন্ধ লেখেন, যাতে তার নদীজলের ডলফিন আবিষ্কারের কথা জানতে পারে সারা পৃথিবী। এই ডলফিনের নাম তিনি দিয়েছিলেন ডেলফিনাস গ্যাঞ্জেটিকাস (কলকাতার বাঙালিরা এই প্রাণীকে বলে শুশুক’)। পরে অবশ্য জানা গেল খ্রিস্টীয় প্রথম শতকেই রোমান পণ্ডিত প্লিনি দ্যা এল্ডার এই ভারতীয় ডলফিনদের বিষয়ে লিখে গেছেন। তাঁর বইয়ে তিনি এই প্রাণীদের প্লাটানিস্টা বলে উল্লেখ করেছেন। এই তথ্য জানার পর পরিবর্তন করা হল রক্সবার্গের দেওয়া নাম। জুওলজিক ইনভেন্টরির তালিকায় এই শুশুকরা এখন প্লাটানিস্টা গ্যাঞ্জেটিকা রক্সবার্গ ১৮০১। বহু বছর পরে, জন অ্যান্ডারসন নামে বটানিকাল গার্ডেনে রক্সবার্গের এক উত্তরসূরি বাথটাবের মধ্যে একটা ডলফিনের বাচ্চা পুষেছিলেন। কয়েক সপ্তাহ বেঁচে ছিল বাচ্চাটা।
“কিন্তু মজার ব্যাপার কী জানেন,” বলল পিয়া, “বাথটাবে ডলফিন পুষলেও অ্যান্ডারসন কিন্তু জানতেন না যে এই প্লাটানিস্টারা চোখে দেখতে পায় না। ওরা যে কাত হয়ে সাঁতার কাটে সেটাও উনি লক্ষ করেননি।”
“তাই বুঝি?”
“হ্যাঁ।”
“সেই বাথটাবটা খুঁজে পেলেন নাকি?” আরও একটু ভাত নেওয়ার জন্য হাত বাড়াল কানাই।
হেসে ফেলল পিয়া। “না। তবে তাতে বিশেষ দুঃখ হয়নি আমার। ওখানে যে যেতে পেরেছি তাতেই আমি খুশি।”
“তো, এর পরে কোথায় গেলেন তীর্থ করতে?” জিজ্ঞেস করল কানাই।
“সেটা শুনলে আরও আশ্চর্য হবেন আপনি,” পিয়া বলল। “সল্ট লেক।”
চোখ কপালে উঠে গেল কানাইয়ের। “মানে, আমাদের সল্ট লেক উপনগরী?”
“উপনগরী তো আর চিরকাল ছিল না,” দ্বিতীয় কলাটার খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে জবাব দিল পিয়া।
“১৮৫২ সালে জায়গাটা ছিল স্রেফ একটা জলা জমি৷ তারই মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কয়েকটা পুকুর আর দিঘি। সে বছর জুলাই মাসে একবার বিশাল এক বান এল,” বলে চলল পিয়া। “ফুলে ফেঁপে উঠল গোটা বদ্বীপের সব নদী। জলের তোড় ঢুকে এল অনেক ভেতর পর্যন্ত। কলকাতার আশেপাশে সমস্ত জলা আর বাদা ভেসে গেল। তারপর জল যখন নামতে শুরু করল, সারা কলকাতায় গুজব ছড়িয়ে গেল শহরের পুবদিকের এক নোনা জলের ঝিলের মধ্যে নাকি এক দল বিশাল সামুদ্রিক জীব আটকা পড়ে রয়েছে। সে সময় কলকাতার বটানিকাল গার্ডেনের সুপারিন্টেডেন্ট ছিলেন ইংরেজ প্রকৃতিবিদ এডওয়ার্ড ব্লিথ। খবরটা শুনে তো তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কারণ ঠিক তার আগের বছরেই মালাবার উপকূলে এভাবে আটকা পড়েছিল একটা তিমি মাছ। সাতাশ মিটার লম্বা সে মাছটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলেছিল সেখানকার গ্রামের লোকেরা। ছুরি, কুড়ুল, বর্শা যে যা পেয়েছিল হাতের কাছে তাই নিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল প্রাণীটার ওপর। ওখানকার এক ইংরেজ পাদরিকে সেই তিমি মাছের টাটকা আর শুকনো মাংস নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছিল লোকে, বলেছিল সে নাকি খুব সুস্বাদু মাংস। এই জীবগুলোকেও যদি ঠিকমতো পরীক্ষা করার আগেই কেটেকুটে খেয়ে নেয় সবাই? এই ভেবে তাড়াতাড়ি সল্ট লেকের দিকে রওনা হলেন ব্লিথ সাহেব।
“প্রাণীগুলোর মরা-বাঁচা নিয়ে সাহেবের যে বিশেষ দুশ্চিন্তা ছিল তা নয়, তবে ওদের মারার কাজটা উনিই নিজের হাতে করতে চেয়েছিলেন, এই যা,” বলল পিয়া।
“আকাশে তখন চড়চড়ে রোদ, গোটা জলাটার থেকে যেন ভাপ উঠছে। বাড়তি বানের জলটাও নেমে গেছে। সল্ট লেকে পৌঁছে সাহেব দেখলেন ছোট একটা এঁদো পুকুরে প্রায় গোটা বিশেক প্রাণী কিলবিল করছে। গোল ধরনের মাথা, সারা শরীর কালো, শুধু পেটের দিকের রংটা সাদা। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ প্রাণীগুলো একেকটা চার মিটারেরও বেশি লম্বা। ডোবাটায় জল তখন এতই কম যে প্রাণীগুলোর সারা শরীর ডুবছে না, পিঠের ছোট পাখনাগুলোর ওপর দুপুরের রোদ পড়ে পিছলে যাচ্ছে। খুবই বিপদে পড়েছে প্রাণীগুলো। এমনকী একটা কাতর আর্তনাদের মতো শব্দও পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। প্রথমটায় ব্লিথের মনে হল ওগুলি বোধহয় খাটো পাখনাওয়ালা পাইলট তিমি, গ্লোবিসেফ্যালাস ডিডাকটর। আটলান্টিক মহাসাগরে এদের বেশি দেখা যায়। বছর ছয়েক আগে ব্রিটিশ শারীরতত্ত্ববিদ জে ই গ্রে এই তিমি আবিষ্কার করেছিলেন। নামকরণটাও গ্রে সাহেবেরই।
“ইনি কি গ্রেজ অ্যানাটমির সেই গ্রে?” কানাই জিজ্ঞেস করল।
“হ্যাঁ। ইনিই তিনি।”
“ডোবাটার চারপাশে ততক্ষণে বহু লোক জড়ো হয়ে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে ব্লিথ দেখলেন তারা কেউ প্রাণীগুলোকে মারে-টারেনি। অনেকে বরং সারা রাত ধরে খাটা-খাটনি করেছে ওদের বাঁচানোর জন্য। সরু একটা খালের মধ্যে দিয়ে টেনে নিয়ে গিয়ে জন্তুগুলোকে নদীতে ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। মনে হল তিমি মাছের মাংসের প্রতি এখানকার গ্রামের লোকেদের বিশেষ আসক্তি নেই। প্রাণীগুলিকে মেরে যে তেল বের করা যেতে পারে সেটাও বোধহয় এদের জানা নেই। ব্লিথ শুনলেন অনেকগুলো প্রাণীকেই এর মধ্যে নদীতে ছেড়ে দিতে পেরেছে গ্রামবাসীরা। বেশ কয়েক ডজনের বড় একটা ঝাক নাকি ছিল এই ডোবায়। তার থেকে এই কয়েকটা এখনও রয়ে গেছে। যে গতিতে উদ্ধারকাজ চলছে, সাহেবের মনে হল খুব বেশি সময় আর হাতে নেই। অবশিষ্ট প্রাণীগুলোর মধ্যে থেকে সব চেয়ে ভাল দেখে দুটোকে বেছে নিলেন ব্লিথ। সঙ্গীদের বললেন পাড়ে খুঁটি পুঁতে । তার সঙ্গে শক্ত দড়ি দড়া দিয়ে সেগুলোকে বেঁধে রাখতে। ভাবলেন পরদিন উপযুক্ত যন্ত্রপাতি নিয়ে এসে ঠিকমতো ব্যবচ্ছেদের বন্দোবস্ত করা যাবে।
“কিন্তু পরদিন সকালে ফিরে এসে সাহেব দেখলেন সব ভো ভা। দুটো তিমির একটাও সেখানে নেই,” পিয়া বলল। “গ্রামের লোকেরা দড়ি কেটে জলে ছেড়ে দিয়েছে তাদের। কিন্তু ব্লিথও দমবার পাত্র নন। শেষ যে ক’টা প্রাণী সেখানে ছিল, তাদের মধ্যে থেকে দুটোকে ডাঙায় তুলে এনে চটপট কেটেকুটে ফেললেন। তারপর দীর্ঘক্ষণ ধরে হাড়গুলোকে পরীক্ষা করে সাহেব সিদ্ধান্তে এলেন এগুলো একেবারে নতুন প্রজাতির প্রাণী। এদের নাম উনি দিলেন ইন্ডিয়ান পাইলট হোয়েল, গ্লোবিসেফ্যালাস ইন্ডিকাস৷
“এইখানে আমার একটা থিয়োরি আছে,” মুচকি হেসে পিয়া বলল। “ব্লিথ যদি সেদিন সল্ট লেকে না যেতেন তা হলে উনিই একদিন ইরাবড়ি ডলফিন আবিষ্কার করতে পারতেন।”
ডান হাতের তর্জনী থেকে একটা ভাতের দানা চেটে নিল কানাই। “কেন?”
“কারণ ছ’বছর পর প্রথম ওর্কায়েলার নমুনাটা যখন উনি দেখলেন, তখন খুব বড় একটা ভুল করে ফেললেন ব্লিথ সাহেব।”
“সেটা আবার কোথায় দেখলেন উনি?”
“কলকাতায়। একটা মাছের বাজারে,” হেসে বলল পিয়া। “কেউ এসে ওনাকে বলেছিল, এরকম একটা অদ্ভুত প্রাণী বাজারে এসেছে। খবরটা শুনে তো দৌড়ে গেলেন সাহেব সেখানে। প্রাণীটাকে এক নজর দেখেই সিদ্ধান্ত করলেন ওটা আসলে একটা বাচ্চা পাইলট তিমি। ছ’বছর আগে সল্ট লেকে যে প্রাণীগুলোকে দেখেছিলেন, সেই জাতের। ওই সল্ট লেকের প্রাণীগুলোকে কিছুতেই মাথা থেকে বের করতে পারেননি ব্লিথ।”
“তা হলে আপনার এই সাধের ডলফিনদের আবিষ্কারকর্তা ব্লিথ সাহেব নন?” জিজ্ঞেস করল কানাই।
“নাঃ,” বলল পিয়া। “একটুর জন্যে সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে গেল ব্লিথবাবুর। তার প্রায় বছর পঁচিশেক পরে কলকাতা থেকে সাড়ে ছ’শো কিলোমিটার দূরে বিশাখাপত্তনমে আরেকটা এই রকম ছোট মাপের গোল-মাথা জলজন্তুর দেহ পাওয়া গেল। এবারে তার কঙ্কালটা সোজা নিয়ে যাওয়া হল ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। সেখানে তো হইচই পড়ে গেল। লন্ডনের শারীরতত্ত্ববিদরা কঙ্কালটা পরীক্ষা করলেন। ব্লিথ সাহেব যা দেখতে পাননি, এই পণ্ডিতদের কিন্তু তা চোখ এড়াতে পারল না। দেখা গেল প্রাণীটা মোটেই পাইলট তিমির বাচ্চা নয়। এটা একটা নতুন প্রজাতির জীব–খুনে তিমি ওসিঁস ওর্সার দূর সম্পর্কের আত্মীয়! কিন্তু ওর্সার সঙ্গে অনেক অমিলও আছে। একেকটা খুনে তিমি লম্বায় দশ মিটার পর্যন্ত হতে পারে, কিন্তু এই নতুন প্রাণীটার দৈর্ঘ্য মেরেকেটে আড়াই মিটার। আবার, খুনে তিমিরা মেরু সাগরের হিম ঠান্ডা জলে থাকতে ভালবাসে, কিন্তু তাদের এই আত্মীয়ের পছন্দ নিরক্ষীয় অঞ্চলের উষ্ণ জল–তা সে নোনা জলও হতে পারে, আবার মিঠেও হতে পারে। বিশালকায় ওর্সার তুলনায় এতই নরম-সরম এই প্রাণীটা, যে এর নামকরণের সময় : পণ্ডিতদের একটা ক্ষুদ্রত্ববাচক শব্দ ভেবে বের করতে হল। নাম ঠিক করা হল ওর্কায়েলা–ওর্কায়েলা ব্রেভিরোষ্ট্রিস।
“আপনি বলতে চান এই খুনেলা তিমি একটা ধরা পড়েছিল কলকাতায়, আর-একটা বিশাখাপত্তনমে?” একটু খটকার সুর কানাইয়ের গলায়।
“হ্যাঁ।”
“তা হলে এদের ‘ইরাবড়ি ডলফিন’ বলা হচ্ছে কেন?”
“সে আরেক কাহিনি। এই ইরাবড়ি ডলফিন নামটা দিয়েছিলেন জন অ্যান্ডারসন–সেই যে সাহেব নিজের বাথটাবে শুশুক পোষার চেষ্টা করেছিলেন,” পিয়া বলল। “১৮৭০-এর দশকে অ্যান্ডারসন বার দুয়েক প্রাণিতাত্ত্বিক অভিযানে বার্মা হয়ে দক্ষিণ চিন পর্যন্ত গিয়েছিলেন। ইরাবড়ি নদীর ভাটি বেয়ে তারা যখন যাচ্ছিলেন, সেই সময়ে কোনও ওর্কায়েলা তাঁদের চোখে পড়েনি। উজানের দিকে কিন্তু প্রচুর সংখ্যায় দেখা গেল ডলফিনগুলোকে। নোনা জলের ডলফিন আর মিষ্টি জলের ডলফিনদের মধ্যে শারীরবৃত্তীয় কিছু তফাতও রয়েছে মনে হল। অ্যান্ডারসন সিদ্ধান্তে এলেন, এই নদীর ডলফিনদের নিশ্চয়ই দুটো আলাদা প্রজাতি রয়েছে: ওর্কায়েলা ব্রেভিরোষ্ট্রিস-এর এক তুতো ভাই আমদানি করলেন সাহেব–ওর্কায়েলা ফ্লিউমিনালিস৷ তার হিসেব মতো এই হল ইরাবড্ডি ডলফিন, এশিয়ার সব নদীর আসল বাসিন্দা।
“অ্যান্ডারসনের দেওয়া নামটা রয়ে গেল, কিন্তু তার সিদ্ধান্তটা টিকল না,” বলল পিয়া। “বেশ কয়েকটা কঙ্কাল পরীক্ষা করে গ্রে সাহেব রায় দিলেন দুটো নয়, ওর্কায়েলার একটার বেশি জাত হয় না। এদের মধ্যে এক দল সমুদ্র উপকূলের নোনা জলে থাকতে ভালবাসে, আর এক দল পছন্দ করে নদীর মিষ্টি জল, সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই; আর এটাও ঠিক যে এই দুই দলের মধ্যে কোনও মেলামেশা নেই, কিন্তু শারীরবৃত্তীয় কোনও অমিল এদের মধ্যে নেই। লিনিয়ান সারণিতে এই ডলফিনদের নাম শেষ পর্যন্ত হল ওর্কায়েলা ব্রেভিরোষ্ট্রিস গ্রে ১৮৮৬।
“আয়রনিটা হল ব্লিথ বেচারির কপালে কোনও কৃতিত্বই শেষ পর্যন্ত জুটল না,” পিয়া বলে চলল। “শুধু যে ওর্কায়েলা আবিষ্কারের সুযোগটা ভদ্রলোকের হাত ফসকে গেল তাই নয়, দেখা গেল সল্ট লেকের জলায় আটকে পড়া প্রাণীগুলোকেও চিনতে ভুল করেছিলেন সাহেব। ওগুলো আসলে ছিল খাটো-পাখনা পাইলট তিমিই। গ্রে দেখিয়ে দিলেন গ্লোবিসেফ্যালাস ইন্ডিকাস বলে কোনও প্রাণী জগতে নেই।”
মাথা নাড়ল কানাই। “এরকমই ছিল সে যুগে। ওর্সার তুলনায় ওর্কায়েলা যেমন, লন্ডনের তুলনায় সেরকমই ছিল কলকাতা।”
নিজের প্লেটটা বাসন ধোয়ার সিঙ্কে নিয়ে যেতে যেতে হেসে ফেলল পিয়া। “সন্দেহ মিটেছে? কলকাতা যে জলচর প্রাণীবিদ্যার একটা প্রধান কেন্দ্র ছিল সে কথা বিশ্বাস হচ্ছে এখন?”
একটা হাত তুলে কানের লতিতে আঙুল বোলাল পিয়া। আগেও এ অভ্যাসটা লক্ষ করেছে কানাই। নর্তকীর মতো মাধুর্যময় আবার একই সাথে শিশুর মতো কোমল এ ভঙ্গিটা যতবার দেখে ততবার বুকটা ধক করে ওঠে কানাইয়ের। পরের দিনই চলে যাবে পিয়া, ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল ওর।
প্লেটটা টেবিলের ওপর রেখে হাত ধুতে বাথরুমে গেল কানাই। মিনিটখানেক বাদেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে সিঙ্কের সামনে এসে পিয়ার কনুইয়ের কাছটায় গিয়ে দাঁড়াল।
“আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে, বুঝলেন?”
“কী?” কানাইয়ের চোখের চকচকে ভাব দেখে একটু সতর্ক গলায় বলল পিয়া। “আপনার কালকের এই অভিযানে কীসের অভাব আছে বলুন তো?”
“কীসের?” কানাইয়ের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ঠোঁট চেপে জিজ্ঞেস করল পিয়া। “একজন ট্রান্সলেটরের,” কানাই বলল। “হরেন আর ফকির ওদের দুজনের কেউই ইংরেজি বলতে পারে না, কাজেই একজন অনুবাদক সঙ্গে না থাকলে আপনি ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন কী করে?”
“কেন? গত কয়েক দিন তো আমি দিব্যি চালিয়ে দিয়েছি।”
“কিন্তু তখন তো আপনার সঙ্গে এত মাঝিমাল্লা ছিল না।”
মাথা নেড়ে সায় দিল পিয়া। মনে হল, ঠিকই, কানাই সঙ্গে থাকলে অনেকটাই সুবিধা হবে কাজের। কিন্তু ওর ষষ্ঠেন্দ্রিয় একটা সতর্কবার্তাওপাঠাচ্ছিল। মনের গভীরে কোথায় যেন বোধ হচ্ছিল কানাইয়ের উপস্থিতি ঝামেলাও ডেকে আনতে পারে। একটু সময় নিয়ে বিষয়টা বোঝার জন্য ও জিজ্ঞেস করল, “কিন্তু আপনার তো এখানে কাজ রয়েছে?”
“কাজ বলতে সেরকম কিছু নয়,” বলল কানাই। মেসোর নোটবইটা প্রায় শেষ হয়েই এসেছে। আর ওটা এখানে বসেই যে পড়তে হবে তারও কোনও মানে নেই। লেখাটা আমি সঙ্গেও নিয়ে যেতে পারি। সত্যি বলতে কী, এই গেস্ট হাউসে একটু হাঁপিয়ে উঠেছি আমি। দু-এক দিন বাইরে ঘুরে এলে মন্দ হয় না।”
স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল কানাইয়ের ব্যগ্রতাটা। তা ছাড়াও একটু বিবেক দংশনও যে হচ্ছিল না তাও নয়–কানাইয়ের আতিথেয়তা যে ত্রুটিহীন সেটা তো অস্বীকার করা যাবে না। সে উদারতার কিছুটা প্রতিদান দিতে পারলে এই গেস্ট হাউসে থাকাটা অনেক সহজ হবে ওর পক্ষে, মনে হল পিয়ার।
“ঠিক আছে তা হলে, চলে আসুন,” সামান্য একটু দ্বিধার পর বলল পিয়া। “ভালই হবে আপনি সঙ্গে এলে।”
এক হাত দিয়ে অন্য হাতের তালুতে এক ঘুষি মারল কানাই। “থ্যাঙ্ক ইউ!” কিন্তু উচ্ছ্বাসের এই প্রকাশে নিজেই মনে হল ও একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। অপ্রতিভ ভাবটা ঢাকতে তাড়াতাড়ি বলল, “আমার কতদিনের শখ একটা এক্সপিডিশনে যাওয়ার। যেদিন থেকে জানতে পেরেছি যে ইয়ংহাজব্যান্ডের তিব্বত অভিযানের সময় আমার ঠাকুর্দার কাকা তাঁর সঙ্গে ট্রান্সলেটর হিসেবে গিয়েছিলেন, সেইদিন থেকেই মনে মনে ঠিক করে রেখেছি আমাকেও একদিন একটা অভিযানে যেতেই হবে।”
.
নিয়তি
বইটা সরিয়ে রেখে কুসুমকে জিজ্ঞেস করলাম, “ঠিক কোন জায়গাটায় যাচ্ছি আমরা বল তো? দ্বীপটার নাম গর্জনতলা কেন?”
“গর্জনগাছের জন্য ওই রকম নাম হয়েছে সার। ওখানে অনেক গর্জনগাছ আছে তো।”
“তাই বুঝি?” এই ব্যাপারটা এতক্ষণ আমার মনে আসনি। গর্জন শব্দের অন্য মানেটাই মাথার মধ্যে ঘুরছিল। “তা হলে বাঘের ডাকের জন্য নামটা হয়নি?”
হাসল ওরা। “তাও হতে পারে।”
“কিন্তু গর্জনতলাতে কেন যাচ্ছি আমরা? মানে ওই জায়গাটাতেই কেন যাচ্ছি, অন্য কোথাও কেন নয়?”
“সে আমার বাবার জন্য সার,” বলল কুসুম।
“তোর বাবার জন্য?”
“হ্যাঁ। অনেক বছর আগে ওই দ্বীপটায় এসে বাবা একবার প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল।”
“তাই নাকি? কী হয়েছিল?”
“জিজ্ঞেস করলেন বলে বলছি স্যার। কিন্তু আমি জানি আপনি বিশ্বাস করবেন না, হয়তো হাসবেন।
“সে অনেক কাল হল, আমার জন্মের বহু বহু দিন আগে; বাবা একদিন জেলে ডিঙি নিয়ে একা পড়েছিল ঝড়ে–ভীষণ তুফানে। সেই তুফানের তোড় ফুঁসে ফুঁসে আসে, তার ঝাঁপটের ঘায়ে, নৌকো ভেঙে ভেসে গেল কুটোর মতন। হাবুডুবু খেতে খেতে গাছের এক গুঁড়ি ধরে কোনওমতে বাবা বেঁচে গেল প্রাণে। ঢেউয়ের ধাক্কায় আর জলের টানেতে, গিয়ে পৌঁছল সেই গর্জনতলা। গাছে চড়ে উঠে বসে গামছার পাকে বাঁধল ডালের সাথে নিজের শরীর। হু হু শব্দে ধেয়ে আসে ঝড়ের ঝাঁপট, দু’হাতে আঁকড়ে ধরে বাবা সেই ডাল। আচমকাই থেমে গেল সব তাণ্ডব, নিশ্চুপ হয়ে গেল গোটা জঙ্গল। তুফানের ধাক্কায় নুয়ে পড়া গাছ সব ফের খাড়া হল, শান্ত হল নদী। চাঁদ নেই আকাশেতে, কালিমাখা রাত, নিঝুম আঁধারে চোখ অন্ধ মনে হয়।
“হঠাৎ প্রচণ্ড এক বাজ পড়ে যেন। থরথর কেঁপে ওঠে সব গাছপালা ভীষণ এক গর্জনে। আর তার সাথে নাকে আসে বদগন্ধ, বাবা শিউরে ওঠে। নাম নেওয়া মানা যার সেই জানোয়ার ওত পেতে আছে কোথা শিকারের খোঁজে। আতঙ্কে অজ্ঞান বাবা গাছের ওপরে কোনওমতে ঝুলে থাকে গামছার বাঁধনে। সেই অচেতন স্বপ্নে আসে বনবিবি, বলে, ‘ওরে মুখ, তোর কেন এত ভয়? আমাকে বিশ্বাস কর, এ দ্বীপ আমার। যে মানুষ মনে সাচ্চা, এই জঙ্গলে তার কোনও ভয় নেই, আমি আছি পাশে।
“ভোরের আলো ফুটলেই দেখিস তখন ভাটার সময় হবে। দ্বীপ পার হয়ে উত্তর দিক পানে হেঁটে চলে যাস। নজর রাখিস জলে, অধৈর্য হস নে দেখবি এ জঙ্গলে তুই একা নোস। আমি আছি কাছাকাছি। দূতেরা আমার তোর পাশে পাশে আছে। তারাই আমার চোখ আর কান সেটা মনে রেখে দিস। যতক্ষণ ভাটা চলে সঙ্গ দেবে তারা। তারপর আসবে তোর মুক্তির সময়। জেলে ডিঙি ভেসে যাবে ওই পথ দিয়ে। তোকে নিয়ে গিয়ে তারা পৌঁছে দেবে ঘরে।”
এত সুন্দরভাবে বলা এরকম একটা গল্প শুনে মুগ্ধ না হয়ে উপায় কী? হেসে জিজ্ঞেস করলাম, “এরপর তুই নিশ্চয়ই বলবি যে পরদিন সকালে হুবহু ওই রকমই সব ঘটেছিল?”
“ঘটেছিল তো সার। যেমন যেমন স্বপ্নে দেখেছিল বাবা, ঠিক সেই রকম। পরে একবার ওই দ্বীপে ফিরে গিয়ে বনবিবির একটা থান তৈরি করে এসেছিল বাবা। যতদিন বাবা বেঁচেছিল, প্রতি বছর বনবিবির পুজোর সময়ে সবাই মিলে আমরা গর্জনতলায় আসতাম।”
আমার হাসি পেয়ে গেল। বললাম, “আর ওই দেবীর দূতদেরও নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছিল তোর বাবা?”
“দেখেছিল তো। একটু পরেই আপনি নিজেও দেখতে পাবেন সার,” বলল কুসুম।
এবার হো হো করে হেসে ফেললাম আমি। “আমিও দেখতে পাব? আমার মতো অবিশ্বাসী নাস্তিক? আমার ওপরে কি এত দয়া হবে দেবীর?”
“হ্যাঁ সার,” আমার ব্যঙ্গ উপেক্ষা করে কুসুম বলল। “কোথায় খুঁজতে হবে জানা থাকলে যে কেউই দেখতে পায় বনবিবির দূতদের।”
ছাতার আড়ালে বসে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি। তন্দ্রা ভাঙল কুসুমের ডাকে। পৌঁছে গেছি আমরা গর্জনতলায়।
ধড়মড় করে উঠে বসলাম। এতক্ষণ ধরে এই সময়টার জন্য অপেক্ষা করছি আমি–কখন কুসুমের বিশ্বাসী মনের ভুল ভেঙে দেওয়ার সুযোগ পাব। ভাটা পড়ে গেছে। বাঁকের মুখে খানিকটা জায়গায় স্থির হয়ে আছে জল–ঠিক সেইখানটাতেই এসে থেমেছে আমাদের নৌকো। ডাঙা এখনও খানিকটা দূরে। দূত-টুত বা অন্য কোনও দৈব দৃশ্য কিছুই দেখা যাচ্ছে না কোথাও। নিজের ওপর একটু খুশি না হয়ে পারলাম না। জয়ের আনন্দ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে করতে কুসুমকে জিজ্ঞেস করলাম, “কী রে, কোথায় গেল তোর দেবীর দূতেরা?”
“দেখতে পাবেন সার, একটু সবুর করুন।”
হঠাৎ একটা অদ্ভুত আওয়াজ কানে এল–আমার মনে হল যেন সশব্দে নাক ঝাড়ছে কেউ। সবিস্ময়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম কিছু একটা অদৃশ্য হয়ে গেল জলের তলায়। শেষ মুহূর্তে কালো চামড়ার একটু আভাস শুধু চোখে পড়ল।
“কী ওটা?” আশ্চর্য হয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। “কোথা থেকে এল? কোথায় চলে গেল?”
“ওই যে,” অন্য আরেক দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল ছোট্ট ফকির। “ওইখানে।”
ঘুরে দাঁড়িয়ে আরেকটা ওরকম জীব দেখতে পেলাম আমি। জলের মধ্যে ডিগবাজি খাচ্ছে। একটা তিনকোনা পাখনাও দেখতে পেলাম এক ঝলক। আগে কখনও দেখিনি, কিন্তু বুঝতে পারলাম ওগুলো কোনও এক জাতের ডলফিন হবে। তবে এখানকার নদীতে যে শুশুক দেখেছি আমি, তার সঙ্গে এদের তফাত আছে। শুশুকের পিঠে এরকম কোনও পাখনা হয় না।
“ওগুলো কী? জিজ্ঞেস করলাম আমি। “কোনও এক ধরনের শুশুক নিশ্চয়ই।”
এবার কুসুমের হাসার পালা। “আমি আমার নিজের মতো নাম দিয়েছি ওদের। আমি ওদের বনবিবির দূত বলি।” ওরই জিত। অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই।
যতক্ষণ নৌকোটা ওখানে দাঁড়িয়ে রইল, জন্তুগুলো খেলা করে বেড়াতে লাগল আমাদের চারপাশে। কেন এখানে এসেছে ওরা? এতক্ষণ ধরে একই জায়গায় রয়েছেই বা কেন? জবাব খুঁজে পেলাম না। তারপর হঠাৎ এক সময় দেখলাম একটা ডলফিন জল থেকে মাথা তুলে সোজা আমার দিকে তাকাল। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম কী করে কুসুম এত সহজে জন্তুগুলোকে অন্য কিছু বলে বিশ্বাস করতে পেরেছে। ওর চোখে যা বনবিবির চিহ্ন বলে মনে হয়েছে, আমার কাছে তাই মনে হল কবির চোখের দৃষ্টি। মনে হল সে চোখ যেন আমাকে বলছে :
“বোবা পশু শান্ত ঘাড় উঁচু করে
আমাদের চুলচেরা দেখে নিতে চায়।
এবং তারই আরেক নাম বুঝি নিয়তি…”
.
মেঘা
সকালে একটা সাইকেল ভ্যান ভাড়া করে ফকিরের জোগাড় করা ভটভটিটা দেখতে গেল পিয়া আর কানাই। ইট-বসানো রাস্তা দিয়ে ঝাঁকুনি খেতে খেতে গ্রামের দিকে চলেছে। ভ্যান। পিয়া বলল, “ওই নৌকোর মালিককে আপনি চেনেন বলছিলেন না? কীরকম লোক ও?”
“আমি যখন ছোটবেলায় এখানে এসেছিলাম তখন ওর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল আমার,
কানাই বলল। “ওর নাম হরেন। হরেন নস্কর। খুব যে চিনি সেটা বলা ঠিক হবে না, তবে এটুকু বলতে পারি যে আমার মেসোর সঙ্গে ওর ভালই যোগাযোগ ছিল।”
“আর ফকিরের কে হয় ও?”
“ধর্মবাপ বলতে পারেন,” জবাব দিল কানাই। “ফকিরের মা মারা যাওয়ার পর হরেনের কাছেই থাকত ও।”
বাঁধের গোড়ার কাছে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল হরেন। ফকির দাঁড়িয়ে ছিল পাশে। এক নজর দেখেই হরেনকে চিনতে পারল কানাই–সেই গাঁট্টাগোট্টা চেহারা, চওড়া কঁধ। শরীরে খানিকটা চর্বি জমেছে এই ক’বছরে। ভুড়ি হয়েছে একটু। ফলে বুকের ছাতিটা আগের চেয়েও চওড়া মনে হচ্ছে। বয়েসের সঙ্গে গম্ভীর হয়েছে মুখের ভাঁজগুলি–চোখ দুটো দেখাই যায় না প্রায়। তবে সাথে সাথে একটা ভারিক্কি ভাবও এসেছে চেহারায়। হাবভাবে যূথপতির গাম্ভীর্য। দেখলেই বোঝা যায় এ মানুষটা আশেপাশের সব লোকেদের শ্রদ্ধার পাত্র। পোশাক-আশাকেও স্বাচ্ছল্যের আভাস ডোরাকাটা লুঙ্গিটা সযত্নে মাড় দিয়ে ইস্ত্রি করা, গায়ের জামা ধবধবে সাদা। হাতে ভারী মেটাল স্ট্র্যাপের ঘড়ি, জামার পকেট থেকে একটা সানগ্লাস উঁকি দিচ্ছে।
“আমাকে চিনতে পারছেন হরেনদা?” হাত জোড় করে নমস্কারের ভঙ্গি করল কানাই। “আমি সারের ভাগ্নে।”
“চিনব না কেন?” হরেন নিরুত্তাপ। “বাড়ি থেকে আপনাকে শাস্তি দিয়ে এখানে পাঠানো হয়েছিল সত্তর সালে। সেই আগুনমুখা ঝড়ের বছর। তবে আপনি তো বোধহয় ঝড়ের আগেই ফিরে গিয়েছিলেন।”
“ঠিক বলেছেন। তা আপনার ছেলেমেয়েরা কেমন আছে? তখন তো বোধহয় তিনটি ছিল, তাই না?”
“ওরা নিজেরাই এখন ছেলেপুলের বাপ-মা হয়ে গেছে,” হরেন বলল। “এই যে, এ হল আমার এক নাতি,” স্মার্ট নীল টি-শার্ট আর জিনস পরা একটা ছেলের দিকে ইশারা করল ও। “ওর নাম নগেন। এই সবে ইস্কুল শেষ করেছে। ও-ও যাবে আমাদের সঙ্গে নৌকোয়।”
“বেশ বেশ,” কানাই বলল। “এবার এনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হলেন শ্রীমতী পিয়ালি রায়, বৈজ্ঞানিক। ইনিই আপনার ভটভটিটা ভাড়া করছেন।”
পিয়ার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝোকাল হরেন। বলল, “চলুন তা হলে, ভটভটিটা দেখে নিন একবার।”
হরেনের পেছন পেছন বাঁধের ওপর উঠে এল পিয়া আর কানাই। সামনে নদীর বুকের ওপর ঢোকা লম্বাটে একটা বালির চড়া দেখা যাচ্ছে। এটাই লুসিবাড়ির জেটি। তার পাশে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে হরেনের ভটভটি। তার গলুইয়ের সামনে বড় বড় সাদা অক্ষরে লেখা ‘এম ভি মেঘা।
এমনিতে নজরে ওঠার মতো কিছু নয় নৌকোটা। কেমন একটু অদ্ভুত ভাবে ভেসে আছে জলের ওপর। জায়গায় জায়গায় রং চটে গেছে, এখানে ওখানে বেড়ানো–পুরনো টিনের খেলনার মতো দেখতে খানিকটা। হরেনের কিন্তু ওর ভটভটি নিয়ে গর্বের শেষ নেই। বিশদভাবে তার গুণকাহিনি বর্ণনা করল ও। এ পর্যন্ত নাকি বহু সওয়ারি বয়েছে এই মেঘা। কখনও কেউ মন্দ বলতে পারেনি। কত পিকনিক পার্টিকে নিয়ে গেছে পাখিরালায়, কত বর আর বরযাত্রীকে নিয়ে দূর দূর দ্বীপে পৌঁছে দিয়েছে সেসব গল্প কানাইকে শোনাল হরেন। খুব একটা অবিশ্বাস্য মনে হল না গল্পগুলো। কারণ বাইরে থেকে দেখে জরাজীর্ণ মনে হলেও, জায়গা অনেক আছে নৌকোটায়। একটু গাদাগাদি হলেও, প্রয়োজন হলে যে এ ভটভটিতে অনেক লোক উঠতে পারে সে ব্যাপারে সন্দেহের বিশেষ কোনও কারণ দেখা গেল না। নৌকোর ভেতর দিকটা খানিকটা বড়সড় একটা গুহার মতো। সারি সারি বেঞ্চি পাতা। টানা লম্বা জানালায় হলুদ তেরপলের পর্দা ঝুলছে। গুহার এক প্রান্তে ইঞ্জিন ঘর, আরেক প্রান্তে রান্নার জায়গা। ওপরে একটা ছোট ডেক, সারেঙের ঘর, আর ছোট্ট ছোট্ট দুটো কেবিন। শেষ প্রান্তে টিন দিয়ে ঘেরা একটা বাথরুম। সেখানে মেঝেতে একটা গর্ত ছাড়া আর কিছুই নেই, তবে মোটের ওপর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।
“দেখতে আহামরি কিছু নয়,” স্বীকার করল কানাই। “তবে কাজ চলে যাবে মনে হয়। ওপরের কেবিনদুটোর একটায় আপনি থাকতে পারবেন, আর একটায় আমি। তা হলে ইঞ্জিনের আওয়াজটাও কানে লাগবে না, আর ধোঁয়াও খেতে হবে না।”
“আর ফকির কোথায় থাকবে?” পিয়া জিজ্ঞেস করল।
“ফকির নীচে থাকবে। হরেন আর ওর হেল্পার, মানে ওর নাতির সঙ্গে।”
“ব্যাস, মাত্র দু’জন? আর কোনও লোকজন লাগবে না?” প্রশ্ন করল পিয়া।
“নাঃ। বেশ ফাঁকায় ফাঁকায় যাওয়া যাবে,” বলল কানাই।
আরেকবার সন্দেহের দৃষ্টিতে মেঘার দিকে তাকাল পিয়া। “রিসার্চের পক্ষে আদর্শ নৌকো বলা যাবে না এটাকে, তবে মনে হয় মোটামুটি চালিয়ে নিতে পারব আমি। একটাই শুধু সমস্যা আছে।”
“কী সমস্যা?”
“এই গামলাটায় চড়ে ডলফিনগুলোকে ফলো করব কী করে সেটাই ভাবছি। সরু খাঁড়ি-টাড়িতে তো এটা ঢুকতে পারবে না।”
পিয়ার প্রশ্নটা হরেনকে অনুবাদ করে শোনাল কানাই। হরেনের জবাবটা আবার ইংরেজিতে বলে দিল পিয়াকে : ফকিরের ডিঙিটাও যাবে ওদের সঙ্গে। দড়ি দিয়ে মেঘার সঙ্গে বাঁধা থাকবে ওটা। তারপর পিয়ার কাজের জায়গায় পৌঁছলে ভটভটিটা এক জায়গায় অপেক্ষা করবে, আর পিয়া ফকিরের সঙ্গে ডিঙিতে করে ডলফিনদের পেছন পেছন যেতে পারবে।
“সত্যি?” এই জবাবটাই শুনতে চাইছিল পিয়া। “এই একটা জায়গায় অন্তত ফকির আমার থেকে এগিয়ে।”
“কী মনে হয়? চলবে?” জিজ্ঞেস করল কানাই।
“চলবে না মানে? চমৎকার আইডিয়া,” পিয়া বলল। “ছোট ডিঙিতেই ডলফিনদের ফলো করা বেশি সুবিধার।”
কানাইয়ের মধ্যস্থতায় ভটভটির ভাড়া-টাড়াগুলো ঠিক করা হয়ে গেল চটপট। ভাড়ার খানিকটা অংশ দিতে চাইল কানাই, কিন্তু কিছুতেই রাজি হল না পিয়া। শেষে রফা হল রসদ যা লাগবে তার খরচটা দু’জনে ভাগ করে নেবে। হরেনকে কিছু টাকা তক্ষুনি দিয়ে দেওয়া হল, চাল, ডাল, তেল, চা, মিনারেল ওয়াটার, গোটাদুয়েক মুরগি আর বিশেষ করে পিয়ার জন্য প্রচুর পাউডার দুধ কেনার জন্য।
“ওঃ, এত এক্সাইটেড লাগছে আমার,” গেস্ট হাউসের পথে ফিরতে ফিরতে বলল পিয়া। “মনে হচ্ছে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ি। গেস্ট হাউসে ফিরে আজ সকালেই জামাকাপড়গুলো কেচে ফেলব।”
“আমিও মাসিকে গিয়ে খবরটা দিই। দিনকয়েক যে থাকব না সেটা জানাই। মাসি আবার কী বলবে কে জানে,” কানাই বলল।
.
দরজা খোলাই ছিল। ঘরে ঢুকে কানাই দেখল টেবিলের সামনে বসে আছে নীলিমা, হাতে চায়ের কাপ। হাসিমুখে তাকাল কানাইয়ের দিকে। কিন্তু তারপরেই হাসি মিলিয়ে গিয়ে ভাজ পড়ল কপালে। “কী ব্যাপার রে কানাই? কিছু গণ্ডগোল হয়েছে?”
“না, গণ্ডগোল কিছু হয়নি,” একটু অস্বস্তির সুর কানাইয়ের গলায়। “তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছিলাম মাসি। আমি কয়েক দিন থাকব না।”
“ফিরে যাচ্ছিস নাকি?” আশ্চর্য হয়ে বলল নীলিমা। “এইতো মাত্র এলি, এখনি চলে যাবি?”
“ফিরে যাচ্ছি না গো,” কানাই বলল। “তুমি রাগ কোরো না মাসি, আসলে পিয়া একটা ভটভটি ভাড়া করেছে ওর সার্ভের জন্য। তো, ওর একজন দোভাষীর দরকার।”
“ও, আই সি,” নীলিমা বলল ইংরেজিতে। “তার মানে তুই ওর সঙ্গে যাচ্ছিস?”
নির্মলের স্মৃতি নীলিমার কাছে যে কতখানি, সেটা ভাল করেই জানে কানাই। নরম গলায় তাই বলল, “ভাবছিলাম নোটবইটাও নিয়ে যাব সঙ্গে। অবশ্য যদি তোমার আপত্তি না থাকে।”
“সাবধানে রাখবি তো?”
“নিশ্চয়ই।”
“কতটা পড়লি এ কয়দিনে?”
“অনেকটাই পড়া হয়ে গেছে,” জবাব দিল কানাই। “ফিরে আসার আগেই শেষ হয়ে যাবে মনে হয়।”
“বেশ। এই নিয়ে আর এখন কিছু জিজ্ঞেস করব না তোকে,”নীলিমা বলল। “কিন্তু একটা কথা বল কানাই, ঠিক কোথায় যাচ্ছিস তোরা?”
কানাই মাথা চুলকোতে লাগল। কোথায় যে যাওয়া হচ্ছে সেটা তো ও জানেই না। জিজ্ঞেস করার কথাটাও মাথায় আসেনি। কিন্তু কোনও ব্যাপারেই নিজের অজ্ঞানতা প্রকাশ করাটা স্বভাবে নেই ওর। তাই যে নদীর নাম মুখে এল বলে দিল মাসিকে। “মনে হয় তারোবাঁকি নদী পর্যন্ত যাব আমরা। একেবারে ফরেস্টের ভেতরে।”
“জঙ্গলে যাচ্ছিস?” একটু চিন্তিত চোখে কানাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল নীলিমা।
“তাই তো জানি,” কানাইয়ের গলায় অনিশ্চয়তা।
চেয়ার ছেড়ে উঠে ওর সামনে এসে দাঁড়াল নীলিমা। “কানাই, ভাল করে ভেবেচিন্তে যাচ্ছিস তো?”
“হ্যাঁ, ভাবব না কেন? ভেবেছি তো,” নিজেকে হঠাৎ একটা স্কুলে-পড়া ছেলের মতো মনে হল কানাইয়ের।
“আমার মনে হয় না তুই ভেবেচিন্তে যাচ্ছিস,” নীলিমা কোমরে হাত রাখল। “অবশ্য তোকে দোষ দেওয়াও যায় না। আমি জানি, বাইরের লোকেরা ধারণাই করতে পারে না কী ধরনের বিপদ হতে পারে এখানকার জঙ্গলে।”
“মানে তুমি বাঘের কথা বলছ?” কানাইয়ের ঠোঁটে মুচকি হাসির আভাস। “পিয়ার মতো একটা তাজা সুস্বাদু খাবার মুখের সামনে থাকলে বাঘে আমার দিকে ফিরেও তাকাবে না।”
“কানাই!” এক ধমক দিল নীলিমা। “এটা ঠাট্টার বিষয় নয়। আমি জানি, এই টুয়েন্টিফার্স্ট সেঞ্চুরিতে দাঁড়িয়ে নিজেকে বাঘের শিকার বলে কল্পনা করাটা তোর পক্ষে সহজ নয়, কিন্তু বাঘের অ্যাটাক এই সুন্দরবনে কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। প্রতি সপ্তাহে অন্তত এ রকম দু-তিনটে ঘটনা এখানে ঘটে।”
“সে কী! এত আকছার?” কানাই জিজ্ঞেস করল।
“হ্যাঁ। তার চেয়ে বেশি বই কম নয়। দাঁড়া, একটা জিনিস তোকে দেখাই,” কানাইয়ের কনুই ধরে ঘরের অন্যপ্রান্তে দেওয়ালের গায়ের সারি সারি বইয়ের তাকগুলোর কাছে নিয়ে গেল নীলিমা। “দেখ,” নীলিমা একটা ফাইলের বান্ডিলের দিকে ইশারা করল। “বছরের পর বছর ধরে লোকের মুখে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে আমি এই আনঅফিশিয়াল রেকর্ড রেখে যাচ্ছি। আমার হিসেব মতো প্রতি বছর একশোরও বেশি মানুষ এখানে বাঘের পেটে যায়। এটা কিন্তু শুধু সুন্দরবনের ইন্ডিয়ান অংশটার কথা বলছি আমি। বাংলাদেশের ভাগটাও যদি ধরিস তা হলে বোধহয় সংখ্যাটা দ্বিগুণেরও বেশি গিয়ে দাঁড়াবে। সব মিলিয়ে হিসেব করলে দেখা যাবে প্রতি একদিন অন্তর একটা করে মানুষ বাঘে নেয় এই সুন্দরবনে। অন্তত।”
চোখ কপালে উঠে গেল কানাইয়ের। “বাঘের হাতে যে মানুষ মরে এখানে সেটা জানতাম, কিন্তু সংখ্যাটা এত বেশি সেটা ধারণা ছিল না।”
“সেটাই সমস্যা,” নীলিমা বলল। “কেউই জানে না ঠিক কত লোক বাঘের কবলে পড়ে সুন্দরবনে। কোনও হিসেবই ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত–সরকারি খাতাপত্রে যা হিসেব দেখানো হয়, সংখ্যাটা তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি।”
কানাই মাথা চুলকাল। “এই বাড়াবাড়িটা নিশ্চয়ই রিসেন্ট ব্যাপার। লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার জন্যও তো হতে পারে? হয়তো বাঘের থাকার জায়গায় মানুষের হাত পড়ছে, বা ওরকম কিছু কারণে?”
“কী যে বলিস,” নীলিমা একটু বিরক্ত হল। “শত শত বছর ধরে এইভাবে মানুষ মরছে এখানে। লোকসংখ্যা যখন এখনকার তুলনায় খুবই সামান্য ছিল তখনও একই ঘটনা ঘটেছে। এইটা দেখ,” বুড়ো আঙুলের ওপর ভর দিয়ে ওপরের তাক থেকে একটা ফাইল টেনে নামাল নীলিমা। তারপর নিয়ে গেল নিজের টেবিলে। “দেখ। এখানে দেখ। দেখতে পাচ্ছিস সংখ্যাটা?”
খোলা পাতাটার দিকে তাকিয়ে কানাই দেখল নীলিমা যেখানে আঙুল রেখেছে ঠিক তার ওপরে লেখা রয়েছে একটা সংখ্যা : ৪,২১৮।
“সংখ্যাটা লক্ষ কর কানাই,” বলল নীলিমা। “এটা হল মাত্র ছ’বছরের হিসেব। ১৮৬০ থেকে ১৮৬৬-র মধ্যে এই এতগুলো তোক বাঘের পেটে গিয়েছিল এই নিম্নবঙ্গে। এটা জে. ফেরারের দেওয়া হিসেব। এই ফেরার ছিলেন একজন ইংরেজ প্রকৃতিবিদ। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার’ নামটা ওনারই দেওয়া। একবার কল্পনা কর কানাই–চার হাজারেরও বেশি মানুষ মরেছে মাত্র ছ’বছরে। গড়ে প্রতিদিন দু’জন করে। একশো বছরে সংখ্যাটা তা হলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে একবার ভেবে দেখ।”
“ষাট-সত্তর হাজার।”ভুরু কুঁচকে ফাইলের খোলা পাতাটার দিকে তাকিয়ে রইল কানাই।
“বিশ্বাস করা কঠিন।”
“কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এটা নির্জলা সত্যি,” নীলিমা বলল। “তোমার কী মনে হয় মাসি? কেন এরকম হয়?” জিজ্ঞেস করল কানাই। “কী হতে পারে কারণটা?”
চেয়ারে বসে পড়ল নীলিমা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “জানি না রে কানাই। এত রকম সব থিয়োরি আছে এই নিয়ে, কোনটা যে বিশ্বাস করব বুঝে উঠতে পারি না।”
“তবে একটা বিষয়ে সব তাত্ত্বিকরাই এক মত, এই ভাটির দেশের বাঘের স্বভাবচরিত্র অন্য সব জায়গার বাঘেদের থেকে একেবারে আলাদা,” বলল নীলিমা। অন্যান্য জায়গার বাঘেরা মানুষকে আক্রমণ করে একমাত্র খুব বিপাকে পড়লে–পঙ্গু হয়ে গেলে বা কোনও কারণে অন্য কোনও শিকার ধরতে অক্ষম হয়ে গেলে। কিন্তু ভাটির দেশের বাঘের জন্য সে তত্ত্ব আদৌ খাটে না। স্বাস্থ্যবান বা কমবয়সি বাঘেদেরও এখানে মানুষখেকো হতে দেখা যায়। কারও কারও মতে এর কারণ হল এখানকার অদ্ভুত পরিবেশতন্ত্র–একমাত্র এই জঙ্গলেই বাঘেদের চারণভূমির অর্ধেকের বেশি অংশ প্রতিদিন ডুবে যায় জোয়ারের জলে। জল তাদের ঘ্রাণচিহ্ন ধুয়ে দেয়, ফলে যে প্রবৃত্তিগত ক্ষমতায় বাঘেরা নিজেদের এলাকা চিনে নিতে পারে তা ঘুলিয়ে যায়। সেইজন্যেই এত হিংস্র হয়ে ওঠে এখানকার বাঘেরা। সুন্দরবনের বাঘের হিংস্রতার কারণ সম্পর্কে যে কয়েকটা তত্ত্বের কথা শোনা যায় তার মধ্যে এটাই সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় নীলিমার। কিন্তু এই তত্ত্ব মেনে নিলেও সে ব্যাপারে করার তো কিছু নেই।
বছর কয়েক পর পরই কেউ না কেউ একটা না একটা নতুন তত্ত্ব এনে হাজির করে। আর মাঝে মাঝে তার সাথে থাকে অদ্ভুত সব সমাধানের উপায়। ১৯৮০-র দশকে একবার এক জার্মান প্রকৃতিবিদ বললেন নরমাংসের প্রতি এখানকার বাঘেদের এই আসক্তির সঙ্গে সুন্দরবনে মিষ্টি জলের অভাবের সম্পর্ক আছে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের খুব মনে ধরেছিল সেই থিয়োরি। বাঘেদের জন্য চটপট কয়েকটা মিষ্টি জলের পুকুর খোঁড়া হয়ে গেল জঙ্গলের ভেতরে।
“ভাব একবার কাণ্ডটা!” নীলিমা বলল। “বাঘের জল খাওয়ার জন্য পুকুর! আর সেটা করা হচ্ছে এমন এক জায়গায় যেখানে মানুষের তেষ্টার কথাটা কেউ ভাবেও না!”
সে যাই হোক, এই পুকুর-টুকুর খোঁড়া সবই শেষ পর্যন্ত বৃথা গেল। বিন্দুমাত্র কোনও লাভ হল না। বাঘের আক্রমণ যেমন চলছিল চলতেই থাকল।
“তার কিছুদিন পর এল আরেকটা নতুন থিয়োরি। ইলেকট্রিক শক,” নীলিমার চোখের কোণে চিকচিক করছে হাসি।
“এক বিশেষজ্ঞের মনে হল পাভলভ তার কুকুরদের যেভাবে একটা নিয়মে অভ্যস্ত করেছিলেন, সেই একই পদ্ধতিতে সুন্দরবনের বাঘেরও অভ্যাস পালটে দেওয়া যেতে পারে। মাটি দিয়ে অনেকগুলো প্রমাণ সাইজের মানুষের মূর্তি বানানো হল। তারপর সেগুলোর গায়ে তার জড়িয়ে সেই তার জুড়ে দেওয়া হল গাড়ির ব্যাটারির সঙ্গে। এই বৈদ্যুতিক মানুষ-পুতুলগুলোকে এবার বসানো হল জঙ্গলের মধ্যে বিভিন্ন দ্বীপে। প্রথম প্রথম কিছুদিন মনে হল ওষুধ ধরেছে। লোকের মনে ফুর্তি আর ধরে না। কিন্তু কয়েকদিন পরেই আবার শুরু হল হানা। মূর্তিগুলো যেমন কে তেমন পড়ে রইল, আর আগের মতোই ফের মরতে লাগল মানুষ।
“আরেকবার, এক ফরেস্ট অফিসারের মাথায় এরকমই আরেকটা অদ্ভুত আইডিয়া এল। জঙ্গলে যারা যাবে, তারা যদি মাথার পেছনদিকে একটা মুখোশ পরে নেয় তা হলে কেমন হয়? যুক্তিটা হল–বাঘে তো মানুষকে সাধারণত পেছনদিক থেকে আক্রমণ করে, তাই ওই একজোড়া রং করা চোখকে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখলে নিশ্চয়ই সেখান থেকে পালিয়ে যাবে। এই থিয়োরিটাও সকলের খুব পছন্দ হল। প্রচুর মুখোশ তৈরি করে বিলি করা হল সর্বত্র। সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হল অসাধারণ এক এক্সপেরিমেন্ট শুরু হয়েছে সুন্দরবনে। আইডিয়াটার চিত্রগুণ লোকের বেশ মনে ধরল। একের পর এক টেলিভিশন ক্যামেরা এল, এমনকী কয়েকজন পরিচালক ফিল্মও বানিয়ে ফেললেন গোটাকতক।
“কিন্তু বাঘেদের দিক থেকে আদৌ কোনও সহযোগিতা পাওয়া গেল না। বোঝাই গেল, মুখ আর মুখোশের তফাত ধরতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হচ্ছে না তাদের।”
“মানে তুমি বলতে চাইছ যে এই সবকিছু বুঝে শুনে হিসেব করে শিকার ধরার ক্ষমতা আছে এখানকার বাঘের?” জিজ্ঞেস করল কানাই।
“জানি না রে কানাই। আমি তো পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে এখানে আছি, কিন্তু একবারও বাঘ দেখিনি। দেখতে চাইও না। এখানকার লোকে যেটা বলে সেটা আমি খুব মানিঃ জঙ্গলে বাঘ দেখে সে গল্প বলার জন্য জ্যান্ত ফিরে আসার সম্ভাবনা খুবই কম। সেইজন্যেই তোকে বলছি কানাই, খেয়াল হল আর জঙ্গলে চলে গেলাম, সেরকম করা মোটেই উচিত নয়। যাওয়ার আগে ভাল করে একবার ভেবে দেখিস, সত্যিই তোর যাওয়ার কোনও প্রয়োজন আছে কি না।”
“কিন্তু আমার তো জঙ্গলে যাওয়ার কোনও প্ল্যান নেই,” কানাই বলল। “আমি তো থাকব ভটভটিতে। সেখানে আর বিপদ কেন হবে?”
“ভটভটিতে থাকলে কোনও বিপদ হতে পারে না ভেবেছিস?”
“হ্যাঁ। আমরা তো জলের ওপরে থাকব। পাড় থেকে অনেক দূরে। সেখানে আর কী হবে?
“তা হলে একটা ঘটনার কথা বলি তোকে। ন’বছর আগে এই লুসিবাড়ি থেকেই একবার একটা বাচ্চা মেয়েকে বাঘে নিয়েছিল। পরে দেখা গেল সে বাঘটা পুরো বিদ্যা নদীর মোহনা সাঁতরে এসেছিল এখানে। তারপর শিকার ধরে আবার ফিরে গিয়েছিল মোহনা পেরিয়ে। দূরত্বটা কত জানিস?”
“না।”
“ছয় ছয় বারো কিলোমিটার, যাতায়াত মিলিয়ে। আর সুন্দরবনের বাঘের পক্ষে সেটা কোনও দূরত্বই নয়। একটানা তেরো কিলোমিটার পর্যন্ত সাঁতরে গিয়ে শিকার ধরেছে বাঘ সেরকম ঘটনাও ঘটেছে এখানে। তাই কখনওই ভাবিস না যে জলের ওপর আছিস বলে বিপদের কোনও সম্ভাবনা নেই। নৌকো আর ভটভটিতে বাঘের হানার কথা আকছারই শোনা যায় এখানে। এমনকী মাঝনদীতেও। প্রত্যেক বছর বেশ কয়েকটা ঘটনা ঘটে এরকম।”
“সত্যি?”
“হ্যাঁ,” মাথা নাড়ল নীলিমা। “আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয় তা হলে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের যে-কোনও লঞ্চ দেখলেই বুঝতে পারবি কতখানি ঝুঁকি নিয়ে চলাফেরা করতে হয় এখানে। একেকটা লঞ্চ একেবারে ভাসমান দুর্গের মতো। আমার কবজির মতো ইয়া মোটা মোটা লোহার গরাদ দেওয়া জানালায়। ফরেস্ট গার্ডদের সঙ্গে বন্দুক থাকা সত্ত্বেও এই রকম দুর্ভেদ্য করে বানানো হয় লঞ্চগুলিকে। তোর ওই ভটভটির জানালায় কি কোনও গরাদ-টরাদের বালাই আছে?”
মাথা চুলকাল কানাই। “মনে পড়ছে না ঠিক।”
“কিছু বলার নেই,” বলল নীলিমা। ব্যাপারটা লক্ষ করারই কোনও প্রয়োজন মনে করিসনি তুই। কোন বিপদের মধ্যে পা বাড়াচ্ছিস সেটা তুই বুঝতে পারছিস বলে মনে হচ্ছে না। জন্তু জানোয়ারের কথা যদি ছেড়েও দিই–এইসব ভটভটি আর নৌকোগুলোই তো সবচেয়ে বিপজ্জনক। প্রতি মাসে কোথাও না কোথাও একটা-দুটো নৌকোডুবি লেগেই আছে।”
“তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পার মাসি। কোনওরকম কোনও ঝুঁকি নেব না আমি,” কানাই বলল।
“কিন্তু একটা কথা তুই বুঝতে পারছিস না কানাই। আমার মনে হচ্ছে তুই নিজেই সবচেয়ে বড় ঝুঁকি। অন্য সবাই কোনও না কোনও প্রয়োজনে যাচ্ছে, কিন্তু তুই তো যাচ্ছিস স্রেফ একটা খেয়ালের বশে। জঙ্গলে যাওয়ার কোনও দরকার তো তোর নেই।”
“তা নয়, একটা কারণ আছে–” কিছু না ভেবেই কথাটা বলতে শুরু করেছিল কানাই। সচেতন হতে হঠাৎ থেমে গেল মাঝপথে।
“কানাই? তুই কিছু লুকোচ্ছিস আমার কাছ থেকে?”
“না না, সেরকম কিছু নয়,” কী বলবে ঠিক ভেবে উঠতে না পেরে মাথা নিচু করল কানাই।
তীক্ষ্ণ চোখে বোনপোর দিকে তাকাল নীলিমা। “ওই মেয়েটা, তাই না? পিয়া?” কোনও জবাব দিল না কানাই। মুখ ঘুরিয়ে তাকাল অন্য দিকে। হঠাৎ গলার সুরে প্রচণ্ড শ্লেষ ঝরিয়ে নীলিমা বলল, “তোরা সব এক রকম, তোরা পুরুষরা। তোদের মতো হিংস্র প্রাণীরা যদি মানুষ বলে পার পেয়ে যায় তা হলে বাঘেদের আর কী দোষ?” এত তেতো সুর মাসির গলায় আগে কখনও শোনেনি কানাই।
কানাইয়ের কনুইটা ধরে আস্তে আস্তে দরজার দিকে এগোল নীলিমা। “সাবধান, কানাই খুব সাবধান, বলে রাখলাম।”
.
স্মৃতি
ডলফিনগুলোর সঙ্গে আধঘণ্টাখানেক কাটানোর পর গর্জনতলার দিকে ফের নৌকো বাইতে শুরু করল হরেন। দ্বীপের কাছাকাছি পৌঁছে আমার দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসতে লাগল ও।
“এসে গেলাম প্রায়। ভয়টা এবার টের পাচ্ছেন সার?”
“ভয়?” জিজ্ঞেস করলাম আমি। “ভয় কেন পাব হরেন? তুমি তো সঙ্গে আছ।”
“ভয়টাই তো রক্ষা করে সার। ভয়ই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে এখানে। ভয় না থাকলে বিপদ দুগুণ বাড়ে।”
“তার মানে তোমার ভয় করছে, তাই না?”
“হ্যাঁ সার। বুঝতে পারছেন না আমার মুখ দেখে?”
ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম সত্যিই ওর মুখে অচেনা একটা ছায়া দেখতে পাচ্ছি আমি–একটা সতর্ক সন্ত্রস্ত ভাব, চোখের দৃষ্টিতে একটা বাড়তি তীক্ষ্ণতা। কেমন যেন ছোঁয়াচে সেই গা ছমছমে ভাব। কয়েক মুহূর্ত পরেই আমারও বেশ ভয় ভয় করতে লাগল। হরেনকে বললাম আমিও ভয় পাচ্ছি ওর মতো।
‘হ্যাঁ গো হরেন, টের পাচ্ছি।”
“ভাল সার, খুব ভাল।”
পাড় যখন আর মিটার বিশেক দূরে, হঠাৎ নৌকো বাওয়া বন্ধ করে দাঁড় তুলে নিল হরেন। চোখ বন্ধ করে কী যেন বিড়বিড় করতে শুরু করল, আর নানা রকম অদ্ভুত ইশারা ইঙ্গিত করতে লাগল হাত দিয়ে।
“কী করছে বল তো ও?” কুসুমকে জিজ্ঞেস করলাম আমি।
“আপনি জানেন না সার? ও বাউলে তো, তাই বড় শেয়ালের মুখ বন্ধ করার মন্তর পড়ছে। সে জানোয়ার আমাদের যাতে কোনও ক্ষতি না করে তার ব্যবস্থা করছে ও।”
অন্য সময় হলে হয়তো হেসে ফেলতাম। কিন্তু এখন তো আমি ভয় পেয়েছি : ভয়ের অভিনয় আর করতে হচ্ছে না আমাকে। আমি জানি যে মন্ত্র পড়ে বাঘের মুখ বন্ধ করার ক্ষমতা আসলে হরেনের নেই। যদি থাকত, তা হলে তো মন্ত্র পড়ে ঝড়ও ডেকে আনতে পারত। কিন্তু তা সম্ভব নয়। তবুও ওর অর্থহীন বিড়বিড়ানি শুনে মনে মনে স্বস্তি পেলাম আমি। ও তো কোনও বাহাদুরি দেখানোর চেষ্টা করছে না, জাদুকরের মতো সম্মোহনের ভঙ্গি করছে না, বরং একজন মিস্ত্রির মতো মন দিয়ে নিজের কাজটুকু করছে–শেষবারের মতো আরেকটু প্যাঁচ দিয়ে নিচ্ছে নাট বল্টগুলিতে, কিছু যাতে আলগা না রয়ে যায়। হরেনের এই ভাবটাই অনেকটা আশ্বস্ত করল আমাকে।
“এবার মন দিয়ে আমার কথাটা শুনুন সার,” বলল হরেন। “আপনি তো আগে জঙ্গলে আসেননি, তাই একটা নিয়ম আপনাকে আমি বলে দিচ্ছি। এটা ভুলবেন না।”
“কী নিয়ম হরেন?”
“নিয়মটা হল, পাড়ে যখন উঠবেন, নিজের কোনও অংশ আপনি সেখানে রেখে আসতে পারবেন না। থুতু ফেলতে পারবেন না, পেচ্ছাপ করতে পারবেন না, পায়খানা করতে পারবেন না–যা খেয়ে এসেছেন তা এখানে দিয়ে যেতে পারবেন না। এই নিয়ম যদি না মানেন তা হলে কিন্তু আমাদের সক্কলের বিপদ।”
কেউ হাসেনি, ঠাট্টাও কেউ করেনি আমাকে নিয়ে, কিন্তু কেমন যেন মনে হল হরেনের কথার সুরে একটা হালকা বিদ্রুপের ছোঁয়া রয়েছে।
“না গো হরেন, কাজকম্ম সব সেরেই এসেছি। কোনও চিন্তা নেই। ভয়ে একেবারে অবশ না হয়ে পড়লে কিচ্ছু ছেড়ে যাব না এখানে,” বললাম আমি।
“ঠিক আছে সার। শুধু বলে রাখলাম আপনাকে।”
আবার দাঁড় বাইতে শুরু করল হরেন। ডাঙা আরেকটু কাছে আসার পর এক ধার দিয়ে লাফিয়ে জলে নেমে পাড়ের দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে লাগল নৌকোটাকে। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম ফকিরও নেমে গেল নদীতে হরেনের পেছন পেছন। জল ওর চিবুক ছুঁই-ছুঁই, কিন্তু তার মধ্যেই নৌকোর গায়ে কাধ ঠেকিয়ে ঠেলা দিতে লাগল গায়ের জোরে।
ওরা কিন্তু কেউ অবাক হল না। ওর মা আমার দিকে ফিরে তাকাল। মনে হল ছেলের গর্বে যেন ফেটে পড়ছে। বলল, “দেখেছেন সার? নদী ওর রক্তে আছে।”
মনে হল আমিও যদি বলতে পারতাম এভাবে! মনে হল যে-কোনও মূল্য দিতে রাজি আছি আমি, যদি এইভাবে একবার বলতে পারি আমার রক্তেও তো আছে নদী, সমস্ত পাপের ভার নিয়ে বয়ে চলেছে আমার শিরায় শিরায়। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে নিজেকে আরও বেশি করে বহিরাগত মনে হতে লাগল আমার। তবুও, শেষ পর্যন্ত কাদায় যখন নামলাম, অনুভব করলাম এত দিন ভাটির দেশে থাকা আমার সার্থক হয়েছে। এই গভীর তলতলে পাঁকের মধ্যে পায়ের পাতাদুটোকে কীভাবে ব্যবহার করতে হয় সেটুকু অন্তত শিখিয়েছে আমাকে এই দেশ। হরেন কুসুমদের পেছন পেছন নিরাপদেই পাড় পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছতে পারলাম আমি।
এবার বাদাবনের ভেতরে ঢোকার পালা। হরেন চলেছে সবার আগে, দা দিয়ে ঝোঁপ জঙ্গল সাফ করতে করতে। তার পেছনে কুসুম–মাটির মূর্তিদুটো কাঁধের ওপর ধরা। আর আমি সবার শেষে। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে বেড়াজালের মতো ঘন এই বাদাবনের মধ্যে যদি একটা বাঘ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার ওপরে, আমার তো কোনওদিকে পালাবারও ক্ষমতা থাকবে না। একেবারে খাঁচায়-পোরা তৈরি খাবার পেয়ে যাবে মুখের সামনে।
কিন্তু কোনও অঘটন ঘটল না। একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পৌঁছলাম আমরা। কুসুম এগিয়ে গেল ঠাকুরের থানের দিকে। থান বলতে মাটি থেকে খানিকটা উঁচু একটা বেদি, চারপাশে বাঁশ দিয়ে ঘেরা, আর মাথায় একটা গোলপাতার ছাউনি। সেখানেই বনবিবি আর তার ভাই শা জঙ্গলির মূর্তিগুলি নামিয়ে রাখলাম আমরা। কুসুম খান কয়েক ধূপকাঠি জ্বালাল, আর জঙ্গল থেকে কিছু ফুলপাতা এনে মূর্তি দুটোর পায়ের কাছে রাখল হরেন।
এই পর্যন্ত বেশ স্বাভাবিক ভাবেই চলছিল ঘটনাক্রম, সাধারণ ঘরোয়া পুজোআর্চায় যেমন হয়। ছেলেবেলায় আমাদের বাড়িতেও মাকে এভাবে ঠাকুরপুজো করতে দেখেছি আমি। তফাত শুধু পারিপার্শ্বিকের। কিন্তু তারপরে হঠাৎ সুর করে একটা মন্ত্র বলতে শুরু করল হরেন। ভীষণ আশ্চর্য হয়ে শুনলাম ও বলে চলেছে :
বিসমিল্লা বলিয়া মুখে ধরিনু কলম/ পয়দা করিল যিনি তামাম
আলম * বড় মেহেরবান তিনি বান্দার উপরে/ তার ছানি কেবা
আছে দুনিয়ার পরে *
একেবারে তাজ্জব বনে গেলাম। আমি তো ভেবে এসেছিলাম একটা হিন্দু পুজোতে যাচ্ছি। তারপর এই প্রার্থনার মধ্যে এত আরবি শব্দ শুনে আমার মনের অবস্থাটা কী রকম হল সহজেই কল্পনা করতে পার। কিন্তু ছন্দটা তো নিঃসন্দেহে পাঁচালির। বাড়িতে কি মন্দিরে কত পুজোতে ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি এই একই সরল পয়ার ছন্দের পাঁচালি-পাঠ।
তন্ময় হয়ে শুনছিলাম হরেনের মন্ত্রোচ্চারণ। মূল ভাষাটা বাংলা, কিন্তু এত আরবি-ফারসি শব্দ তাতে মেশানো, যে সবটা ভাল বোঝা যাচ্ছিল না। গল্পটা অবশ্য আমার চেনা : সেই দুখের দুর্দশার কাহিনী। কেমন করে তাকে একটা নির্জন দ্বীপে ব্যাঘ্ৰদানব দক্ষিণ রায়ের মুখে ফেলে চলে আসা হয়েছিল, আর সেখান থেকে কীভাবে বনবিবি আর শা জঙ্গলি তাকে রক্ষা করলেন সেই গল্প।
এক এক করে সকলের পুজো দেওয়া শেষ হল। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে ফাঁকা জায়গাটুকু পেরিয়ে আমরা আবার গিয়ে ডিঙিতে উঠলাম। নৌকো করে মরিচঝাঁপির দিকে যেতে যেতে আমি জিজ্ঞেস করলাম, “এত লম্বা এই মন্ত্র তুমি কোথায় শিখলে হরেন?”
খানিকটা যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ও তাকাল আমার দিকে। “এ তো আমি ছেলেবেলা থেকেই জানি সার। বাবাকে তো শুনতাম এই মন্তর পড়তে, সেই শুনে শুনে শিখেছি।”
“মানে মুখে মুখেই এটা চলে আসছে? শুধু শুনে শুনে মনে রেখে দিতে হয়?”
“তা কেন স্যার?” হরেন বলল। “ছাপা বইও পাওয়া যায়। একখানা আমার কাছেও আছে।” নিচু হয়ে নৌকোর খোলের ভেতরে অন্যান্য জিনিসপত্রের মধ্যে থেকে হলদে হয়ে যাওয়া ছেঁড়া একটা চটি বই বের করে আনল ও। “এই যে সার, দেখুন।”
প্রথম পাতায় দেখলাম বইয়ের নাম লেখা আছে বনবিবির কেরামতি অর্থাৎ বনবিবি জহুরানামা। বইটা খুলতে গিয়েই কিন্তু একটা ধাক্কা খেলাম : এ তো আরবি কেতাবের মতো ডাইনে থেকে বাঁয়ে পাতা উলটে পড়তে হয়, বাংলা বইয়ের মতো বদিক থেকে ডাইনে নয়। ছন্দপ্রকরণ যদিও বাংলা লোককথার ধরনের : দ্বিপদী পয়ারে লেখা। দুটো করে লাইনের একেকটা শ্লোক–এক এক লাইনে মাত্রা সংখ্যা মোটামুটি বারো, আর প্রতি লাইনের মাঝামাঝি জায়গায় একবার করে যতি।
বইটা দেখলাম একজন মুসলমান ভদ্রলোকের লেখা। লেখকের নাম দেওয়া আছে আব্দুর রহিম। সাধারণ মাপকাঠিতে বিচার করলে খুব একটা সাহিত্যগুণসমৃদ্ধ বলা চলে না লেখাটাকে। প্রতি জোড়া লাইনে মোটা দাগের একটা ছন্দমিল যদিও আছে, কিন্তু পুরো লেখাটা দেখতে আদৌ কবিতার মতো নয়। গদ্যের মতো একটানা। মাঝে মাঝে শুধু তারা চিহ্ন আর দুই দাড়ি দেওয়া। অন্য ভাবে বলতে গেলে লেখাটা দেখতে গদ্যের মতো কিন্তু পড়তে পদ্যের মতো–অদ্ভুত একটা মিশ্রণ, প্রথমটায় মনে হল আমার। তার পরে আস্তে আস্তে বুঝতে পারলাম বিষয়টার অসাধারণত্ব। গদ্য এখানে ছন্দ আর তালের সিঁড়িতে ভর করে পদ্যের জগতে উত্তীর্ণ হচ্ছে–এক কথায় চমৎকার।
“কবে লেখা হয়েছে এ বইটা?” আমি জিজ্ঞেস করলাম হরেনকে। “তুমি জানো?”
“এ তো পুরনো বই স্যার। অনেক, অনেক পুরনো।”
অনেক, অনেক পুরনো? কিন্তু প্রথম পাতাতেই তো দেখতে পাচ্ছি এক জায়গায় লেখা আছে, “কেহ দিবা নিশি চলে আতলস পরিয়া/ ছায়ের করিয়া ফেরে চৌদ্দলে চড়িয়া।”
হঠাৎ মনে হল এই কাহিনির জন্ম নিশ্চয়ই উনিশ শতকের শেষে অথবা বিশ শতকের প্রথম দিকে, যখন নতুন বাসিন্দারা সবে আসতে শুরু করেছে এই ভাটির দেশে। সে কারণেই হয়তো লোককথা আর ধর্মশাস্ত্র, নিকট আর দূর, বাংলা আর আরবির মিশ্রণে এরকম আশ্চর্য চেহারা নিয়েছে এই জহুরানামা। কে বলতে পারে?
অবশ্য কী-ই বা হতে পারে তা ছাড়া? নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে তোত আমি দেখেছি–শুধু পলি বয়ে আনা নদীর ঢেউ ছাড়াও, কাছের দূরের নানা ভাষার স্রোত বার বার এসে আছড়ে পড়েছে এই ভাটির দেশে, এখানকার মাটিতে মিশে আছে। তাদের চিহ্ন। বাংলা, ইংরেজি, আরবি, হিন্দি, আরাকানি–আরও কত ভাষা কে জানে। এক ভাষার স্রোত গিয়ে মিশেছে অন্য ভাষায়, জন্ম দিয়েছে সেই প্রবাহে ভাসমান অগুন্তি ছোট ছোট ভাষা জগতের। চৈতন্যোদয় হল আমার : এ ভাটির দেশে মানুষের বিশ্বাসও এখানকার বিশাল সব মোহনার মতো। সে মোহনা শুধু অনেক নদীর মিলনের জায়গাই নয়, সে হল বহু পথের সংযোগস্থল। সে সব পথ নানা দিকে টেনে নিয়ে যায় মানুষকে–এক দেশ থেকে অন্য দেশে, এমনকী এক বিশ্বাস থেকে আরেক বিশ্বাসে, এক ধর্ম থেকে অন্য ধর্মে।
বিষয়টা মাথায় এমন চেপে বসল যে তক্ষুনি কাঁধের ঝোলা থেকে নোটবই বের করে কয়েকটা লাইন টুকতে শুরু করে দিলাম আমি। ঘটনাচক্রে এই নোটবইটাই ছিল সেদিন আমার সঙ্গে। খুদে খুদে ছাপার অক্ষর, চোখ কুঁচকে বেশ কষ্ট করে পড়তে হচ্ছিল আমাকে। এক সময় অন্যমনস্ক ভাবে ফকিরের হাতে তুলে দিলাম চটি বইটা–অনেক সময় ক্লাসে ছাত্রদের যেমন দিতাম–বললাম, “জোরে জোরে পড়ো, লিখে নিই।”
ও জোরে জোরে উচ্চারণ করতে থাকল শব্দগুলো, আর আমি লিখতে শুরু করলাম। লিখতে লিখতে হঠাৎ একটা কথা খেয়াল হল আমার। কুসুমকে বললাম, “আচ্ছা, তুই না বলেছিলি ফকির লিখতে পড়তে পারে না?”
“হ্যাঁ সার। ও তো লেখাপড়া শেখেনি,” জবাব দিল কুসুম। “তা হলে?”
একটু হেসে ফকিরের মাথায় হাত বুলিয়ে দিল কুসুম। “এটা তো ওর মুখস্থ। এত বার আমার কাছ থেকে শুনেছে যে কথাগুলো ওর মাথায় গেঁথে গেছে একেবারে।”
.
সন্ধে হয়ে গেছে। আমার লেখার যাতে অসুবিধা না হয় সে জন্য সামনে একটা মোমবাতি রেখে গেছে কুসুম। ওদিকে হরেন অধৈর্য হয়ে উঠছে। ফকিরকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পড়েছে ওর ওপর। শুধু কুসুম আর আমি এখন থাকব এখানে। জলের ওপর থেকে ভেসে আসছে টহলদার নৌকোর শব্দ। গোটা দ্বীপটাকে ঘিরে ফেলেছে নৌকোগুলো। অন্ধকার আর একটু গাঢ় না হলে ফকিরকে নিয়ে পালাতে পারবে না হরেন।
কিন্তু আর সবুর সইছে না হরেনের। এখনই বেরোতে চায় ও। আমি বললাম, “আর কয়েকটা ঘণ্টা অপেক্ষা করো। সারাটা রাত তো পড়েই রয়েছে।” আমার সঙ্গে গলা মেলাল কুসুমও। হরেনকে ডেকে নিয়ে গেল বাইরে : “চলো, তোমার নৌকোয় যাই। সারকে একটু একা থাকতে দাও।”
.
মধ্যস্থ
নোটপত্র গোছানো, জামাকাপড় কাঁচা আর যন্ত্রপাতি পরিষ্কারের কাজ শেষ হতে হতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নেমে গেল। পিয়া ঠিক করল এখনই শুয়ে পড়বে। রাতের খাওয়ার জন্য আর অপেক্ষা করবে না। এরপরে কবে আবার কপালে একটা বিছানা জুটবে তার তো কোনও ঠিক নেই। তাই আজকে রাতে এই বিছানাটার সদ্ব্যবহার করাই ভাল। যতটা পারা যায় ঘুমিয়ে নেবে ও। কানাই ছাদের স্টাডিতে পড়াশোনা করছে, ওকে আর খামখা ডিস্টার্ব করার দরকার নেই। এক গ্লাস ওভালটিন গুলে নিয়ে নীচে ফাঁকায় নেমে এল পিয়া।
চাঁদ উঠে গেছে অনেকক্ষণ। রুপোলি আলোয় পিয়া দেখতে পেল নীলিমা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মনে হল কী যেন একটা গভীর চিন্তায় ডুবে আছে। পিয়ার পায়ের শব্দ পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল।
এক হাতে ওভালটিনের গ্লাস, অন্য হাতটা দিয়ে বাতাসে ঢেউয়ের মতো একটা আঁক কাটল পিয়া : “হ্যালো।”
জবাবে একটু হাসল নীলিমা। কী যেন বলল বাংলায়। খানিকটা আপশোসের সুরে পিয়া বলল, “সরি। বুঝতে পারলাম না।”
“আরে, তাই তো,”নীলিমা বলল। “আমারই তো সরি বলা উচিত। বার বার খালি ভুলে যাই আমি। আসলে তোমার চেহারাটার জন্যই একটুও খেয়াল থাকে না আমার। খালি নিজেকে মনে করাতে থাকি যাতে বাংলা না বলি তোমার সঙ্গে, তাও ঠিক বেরিয়ে যায় মুখ ফসকে।”
হাসল পিয়া। “আমার মা বলত বাংলা ভাষাটা না-জানার জন্য একদিন দুঃখ করব আমি। মনে হয় ঠিকই বলত মা।”
“কিন্তু একটা কথা বলো তো বাছা,” নীলিমা বলল, “জানতে ইচ্ছে করছে বলেই জিজ্ঞেস করছি–তোমার বাবা-মা কেন তোমাকে কখনও বাংলা শেখাতে চেষ্টা করেননি?”
“মা একটু চেষ্টা করেছিল,” বলল পিয়া। “আমারই বিশেষ আগ্রহ ছিল না। আর বাবার কথা যদি বলেন, তা হলে মনে হয় বিষয়টা নিয়ে বাবার নিজের মনেই একটু সন্দেহ ছিল।
“সন্দেহ? তোমাকে বাংলা শেখানোর ব্যাপারে?”
“হ্যাঁ,” পিয়া বলল। “পুরো গল্পটা একটু কমপ্লিকেটেড। আসলে আমার ঠাকুরদা-ঠাকুরমাও ছিলেন প্রবাসী বাঙালি–বার্মায় থাকতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সেখানকার ঘরবাড়ি ছেড়ে ওদের দেশে ফিরে আসতে হয়েছিল। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে বড় হবার ফলে প্রবাসী বা উদ্বাস্তুদের বিষয়ে নিজের মতো করে কয়েকটা থিয়োরি তৈরি করে নিয়েছিল বাবা। বাবার ধারণা হল ভারতীয়রা বিশেষ করে বাঙালিরা কখনওই ভাল পর্যটক হতে পারে না। কারণ তাদের চোখ সব সময় ফেরানো থাকে পেছন দিকে ঘরের দিকে। তাই যখন আমরা আমেরিকায় গেলাম, বাবা ঠিক করল যে এই ভুল করবে না। সে দেশের মতো করেই খাপ খাইয়ে নেবে নিজেকে।”
“তাই উনি তোমার সঙ্গে সব সময় ইংরেজিতে কথা বলতেন?”
“হ্যাঁ,” পিয়া বলল। “আর এর জন্যে অনেকটাই ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল বাবাকে, সেটা ভুললে চলবে না। কারণ ইংরেজি ভাষাটা খুব ভাল বলতে পারত না বাবা। এখনও, এই এতদিন বিদেশে থাকার পরেও পারে না। বাবা পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, ফলে কথা যখন বলে ইংরেজিটা খানিকটা যেন কন্সট্রাকশন ম্যানুয়েলের মতো শোনায়।”
“তোমার মায়ের সঙ্গে কী ভাষায় কথা বলতেন উনি?”
“নিজেদের মধ্যে বাবা-মা বাংলাই বলত,” হেসে বলল পিয়া। অবশ্য যখন ওরা কথা বলত। আর দু’জনের মধ্যে কথা যখন বন্ধ থাকত তখন আমিই ছিলাম ওদের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। তবে এই বার্তাবাহকের কাজ করার সময় বাবা-মাকে ইংরেজিতে কথা বলতে বাধ্য করতাম আমি–তা না হলে কিছুতেই খবর পৌঁছে দিতাম না।”
কোনও জবাব দিল না নীলিমা। একটু অস্বস্তি হল পিয়ার। ভুল করে কোনও বেফঁস কথা বলা হয়ে গেল নাকি? কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই নিজের আঁচলের কোনাটা ধরে মুখের কাছে নিয়ে গেল নীলিমা। দু’চোখে টলটল করছে জল।
“আই অ্যাম সরি,” তাড়াতাড়ি বলল পিয়া। “আমি কি অন্যায় কিছু বলে ফেলেছি?”
“না বাছা। অন্যায় কিছু বলনি। আমি খালি তোমার ছোটবেলার কথা ভাবছিলাম–কেমন করে বাবা-মার কথাগুলো পৌঁছে দিতে পরস্পরের কাছে। স্বামী-স্ত্রী যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলতে পারে না সেটা যে কত দুঃখের কথা সে তোমাকে কী বলব বাছা। তাও তো তুমি ছিলে তোমার বাবা-মার মাঝখানে। যদি কেউ না থাকত তা হলে–”
কথাটা শেষ করল না নীলিমা। থেমে গেল আবার। পিয়া বুঝতে পারছিল ব্যক্তিগত কোনও ব্যথার জায়গায় ছুঁয়ে ফেলেছে না বুঝে। নীলিমার ধাতস্থ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল চুপ করে।
“আমাদের বাড়িতে তো ছেলেপুলে বলতে ওই কানাই-ই একবার এসে ছিল কিছুদিনের জন্য,” অবশেষে বলল নীলিমা। “আমার স্বামীর কাছে সেইটুকুই যে কতখানি ছিল সেটা আগে আমি কল্পনাও করতে পারিনি। শুধু নিজের কথাগুলো কাউকে বলে যাওয়ার জন্যেই যে কী আকুলতা ছিল মানুষটার, কী বলব। তারপরেও কত বছর ধরে যে আমাকে বলেছে, কানাইটা যদি আবার এসে কিছুদিন থাকত। আমি মনে করিয়ে দিতাম, কানাই তো আর ছোটটি নেই, বড় হয়ে গেছে। তারও নিজের কাজকর্ম আছে। কিন্তু তাতে কিছু এসে যেত না আমার স্বামীর। কতবার যে চিঠি লিখেছে কানাইকে, এখানে আসার জন্য।”
“কানাই আসেনি?”
“নাঃ,” একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল নীলিমা। “ও তখন খুবই ব্যস্ত। ব্যবসায় উন্নতি করছে। তার দামটাও তো দিতে হবে। নিজের জন্যে ছাড়া আর কারও জন্যেই সময় ছিল না ওর। নিজের মা-বাবার জন্যেও না। আমাদের কথা তো ছেড়েই দাও।”
“ও কি সব সময়ই এই রকম?” পিয়া জিজ্ঞেস করল। “এই রকম উদ্যমী?”
“কেউ কেউ বলে স্বার্থপর,” জবাব দিল নীলিমা। “আসলে কানাইয়ের মুশকিলটা কী জানো তো? ও সব সময়ই একটু বেশি চালাক। সব কিছু খুব সহজেই হাতে এসে গেছে তো, তাই বেশির ভাগ মানুষের কাছে দুনিয়াটা যে কী রকম সে বোধটাই ওর কখনও হয়নি।”
পিয়া বুঝতে পারল তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী নীলিমা ঠিকই চিনেছে তার ভাগ্নেকে। কিন্তু সে ধারণাটা প্রকাশ না করাই ভাল মনে হল। ভদ্রতা রাখতে বলল, “আমি তো ওকে সামান্যই দেখেছি, আমি আর কী বলব?”
“ঠিকই,” বলল নীলিমা। “তবে তোমাকে একটু সাবধান করে দিই বাছা। আমার ভাগ্নেকে আমি ভালবাসি ঠিকই, কিন্তু একটা কথা আমার বলে দেওয়া উচিত যে কানাই হল সেই ধরনের মানুষ যারা মনে করে যে মেয়েরা তাদের কাছাকাছি এলেই প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খাবে। দুঃখের বিষয় হল পৃথিবীতে বোকা মেয়ের তো অভাব নেই। অনেকেই আছে যারা এই রকম লোকেদের ধারণাকে সত্যি বলে প্রমাণ করে। কানাই মনে হয় সব সময় সেই রকম মেয়েদেরই খুঁজে বেড়ায়। তোমরা কী বল জানি না, আমাদের সময় তো এ ধরনের লোকেদের আমরা বলতাম লম্পট’।” নীলিমা কথা শেষ করল। ভুরু উপরে তুলে জিজ্ঞেস করল, “আমার কথাটা বুঝতে পেরেছ তো?”
“বুঝেছি।”
মাথা নেড়ে শাড়ির আঁচলে নাক মুছল নীলিমা। “যাকগে, আর ভ্যাজর ভ্যাজর করব না। কাল তো তোমার অনেক কাজ, তাই না?”
“হ্যাঁ,” বলল পিয়া। “আমরা সকাল সকালই বেরিয়ে পড়ব। সত্যি, ভাবতেই ভাল লাগছে।”
পিয়ার কাঁধের ওপর একটা হাত দিয়ে ওকে বুকের কাছে টেনে নিল নীলিমা। “শোনো বাছা, খুব সাবধানে থাকবে। জঙ্গল ভয়ংকর জায়গা, মনে রাখবে। আর সব সময় জন্তু জানোয়াররাই যে শুধু ভয়ের কারণ তা কিন্তু নয়।”
.
ঘেরাটোপে
আমি গর্জনতলা থেকে ঘুরে আসার কয়েকদিন পর নীলিমা ফিরল তার কাজ শেষ করে। সঙ্গে নিয়ে এল বাইরের পৃথিবীর অজস্র খবর। নানা গল্প করতে করতে এ কথা সে কথার মাঝখানে হঠাৎই বলল, “আর মরিচঝাঁপিতেও মনে হয় এবার কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।”
আমার কান খাড়া হয়ে উঠল। “কী ঘটতে যাচ্ছে?”
“মনে হয় সরকার এবার ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত করতে চায়। সেরকম দরকার হলে কঠিন ব্যবস্থা নেওয়া হবে ঠিক হয়েছে শুনলাম।”
কিছু বললাম না, শুধু মনে মনে ভাবতে লাগলাম কী করে খবরটা পৌঁছে দেওয়া যায় কুসুমের কাছে, কী করে সাবধান করে দেওয়া যায় ওদের। কিন্তু খুব দ্রুত ঘটনা গুরুতর মোড় নিল। সাবধান করে দেওয়ার কোনও পথই রইল না। পরদিন শোনা গেল বন সংরক্ষণ আইনে মরিচঝাঁপিতে যাতায়াত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে সরকার। পুরো এলাকায় জারি করা হয়েছে ১৪৪ ধারা। তার মানে চারজনের বেশি লোক এক জায়গায় জড়ো হওয়াও নিষিদ্ধ।
বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নদী বেয়ে স্রোতের মতো ছড়িয়ে যেতে শুরু করল নানা গুজব। শোনা গেল কয়েক ডজন পুলিশের নৌকো ঘিরে রেখেছে গোটা দ্বীপটাকে, কাদানে গ্যাস আর রাবার বুলেট চালানো হয়েছে, দ্বীপে কোনও খাবার-দাবার বা জল নিয়ে যেতে দেওয়া হচ্ছে না মরিচঝাঁপির লোকেদের, বেশ কয়েকটা নৌকো ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে, কয়েক জন নাকি মারাও গেছে। সময় যত যেতে লাগল গুজবগুলিও তত ফুলেফেঁপে উঠতে থাকল; মনে হল যেন যুদ্ধ লেগেছে শান্ত নিরিবিলি এই ভাটির দেশে।
নীলিমার কথা ভেবেই প্রাণপণে স্থির থাকার চেষ্টা করছিলাম আমি। মনের মধ্যে যে উথাল পাথাল চলছিল তাকে বাইরে প্রকাশ হতে দিচ্ছিলাম না। কিন্তু সেদিন সারারাত কিছুতেই দু’চোখের পাতা এক করতে পারলাম না। সকাল হতেই মনে মনে বুঝলাম মরিচঝাঁপিতে যেতে আমাকে হবেই। যে-কোনও উপায়েই থোক। তার জন্যে এমনকী নীলিমার সঙ্গে বিবাদে যেতেও আমি প্রস্তুত। আমার সৌভাগ্য, পরিস্থিতি সেদিকে যায়নি–অন্তত এখনও পর্যন্ত নয়। ভোরবেলায় স্কুলের কয়েকজন মাস্টারমশাই এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। তাঁদেরও কানে এসেছে গুজবগুলো, আর আমারই মতো তারাও চিন্তায় আছেন ওই দ্বীপবাসীদের জন্য। এতটাই উদ্বিগ্ন তাঁরা, যে একটা ভটভটি পর্যন্ত ভাড়া করে ফেলেছেন মরিচঝাঁপি যাওয়ার জন্য : যদি কোনওভাবে মিটমাটের একটা রাস্তা বের করা যায়। মাস্টারমশাইরা জিজ্ঞেস করলেন আমিও তাঁদের সঙ্গে যেতে রাজি আছি কি না। আমি তো এক পা তুলে খাড়া।
সকাল দশটা নাগাদ ছাড়ল আমাদের ভটভটি। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দূর থেকে দেখা গেল আমাদের গন্তব্য। এখানে একটা কথা বলে রাখি–মরিচঝাঁপি বিশাল দ্বীপ, ভাটির দেশের সবচেয়ে বড় দ্বীপগুলির একটা। এখানকার তটরেখার দৈর্ঘ্য প্রায় কুড়ি কিলোমিটার। প্রথম যখন চোখে পড়ল দ্বীপটা, তখনও আমরা প্রায় দু-তিন কিলোমিটার দূরে। দেখলাম ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে দ্বীপের ওপর।
খানিক পরেই দেখা গেল সরকারি মোটরবোটগুলিকে। টহল দিচ্ছে দ্বীপের চারপাশে। আমাদের ভটভটিওয়ালা দেখলাম বেশ ভয় পেয়ে গেছে। অনেক কাকুতি-মিনতি করে তাকে আরেকটু কাছাকাছি যেতে রাজি করানো গেল। রাজি সে হল বটে, কিন্তু একটা শর্তে : আমাদের নৌকো যাবে নদীর অন্য পাড় ধরে–দ্বীপ থেকে যতটা সম্ভব দূরত্ব বজায় রেখে। অতএব সে ভাবেই এপাশের কিনারা ঘেঁষে এগোতে লাগলাম আমরা, আর আমাদের দৃষ্টি ফেরানো রইল অন্যদিকে, মরিচঝাঁপির দিকে।
এভাবে চলতে চলতে একটা গ্রামের কাছাকাছি এসে পৌঁছলাম আমরা। দেখতে পেলাম পাড়ের ওপর বহু লোক জড়ো হয়েছে, ব্যস্তসমস্ত ভাবে তারা একটা নৌকোয় প্রচুর মালপত্র বোঝাই করছে। ভটভটি বা পালের নৌকো নয় কিন্তু, এমনি সাধারণ ডিঙি নৌকো, হরেনের যেরকম একটা ছিল। খানিকটা দূর থেকেও দিব্যি বোঝা গেল নৌকোটাতে রসদ বোঝাই করছে ওরা–বস্তা বস্তা চাল-ডাল আর জেরিক্যান ভর্তি খাবার জল। তারপর এক এক করে অনেকে গিয়ে উঠে পড়ল নৌকোটাতে। বেশিরভাগই পুরুষ, তবে কিছু মহিলা এবং বাচ্চাও ছিল। কয়েকজন তো বোঝাই যাচ্ছিল দিনমজুর–কাজের জন্য গিয়েছিল অন্য কোনও দ্বীপে, তারপরে আর ফিরতে পারেনি। বাকিরা মনে হল কোনও কারণে আত্মীয়স্বজনদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, আর এখন যে-কোনও রকমে ফেরার চেষ্টা করছে মরিচঝাঁপিতে। তবে কারণ যাই হোক না কেন, ওদের গরজটা বেশ বোঝা যাচ্ছিল। গাদাগাদি করে এই রকম একটা পলকা ডিঙিতে ওঠার ঝুঁকি নিতেও তাই দ্বিধা ছিল না ওদের। অবশেষে নৌকো যখন ছাড়ল তখন তাতে অন্তত ডজন দুয়েক লোক। কোনও রকমে টলমল করতে করতে স্রোতের মুখে গিয়ে পড়ল ডিঙিটা। টইটম্বুর ভর্তি ওইটুকু একটা মোচার খোলা–কীভাবে যে ভেসে ছিল না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। খানিকটা দূর থেকে রুদ্ধশ্বাসে আমরা দেখতে লাগলাম। সকলেরই বুক দুরুদুরু–কী হয় কী হয়। বোঝাই যাচ্ছিল ওদের আশা পুলিশকে এড়িয়ে কোনও রকমে পৌঁছতে পারবে মরিচঝাঁপিতে, আটকা-পড়া দ্বীপবাসীদের কাছেও পৌঁছে দেবে কিছু রসদ। এখন পুলিশ কী করবে? আমাদের নৌকোয় প্রত্যেকেরই দেখলাম এ ব্যাপারে নিজস্ব কিছু বক্তব্য রয়েছে।
হঠাৎ, ঠিক যেন আমাদের সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটানোর জন্যই, বাগনা নদী বেয়ে গর্জন করতে করতে ধেয়ে এল একটা পুলিশের স্পিডবোট। তিরবেগে ডিঙিটার কাছে পৌঁছে তার চারদিকে পাক খেতে লাগল সেটা। পুলিশের বোটে দেখা গেল একটা লাউডস্পিকার আছে। যদিও আমরা বেশ খানিকটা দূরেই ছিলাম, মাইকে পুলিশ কী বলছে তার দু-একটা টুকরো ঠিকই কানে এসে পৌঁছচ্ছিল। ডিঙির মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে যেখান থেকে এসেছে আবার সেখানেই ফেরত যেতে বলছিল ওরা। জবাবে নৌকোর লোকেরা কী বলল সেটা শুনতে পেলাম না, কিন্তু ভাবভঙ্গি দেখে বোঝা যাচ্ছিল পুলিশগুলোকে মিনতি করছে ওরা, বলছে ওদের যেতে দিতে মরিচঝাঁপিতে।
ফল হল উলটো। পুলিশের লোকগুলো ভয়ানক খেপে চিৎকার করতে লাগল। মাইকে। আচমকা, বাজ পড়ার মতো, একটা বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল। শূন্যে গুলি ছুঁড়েছে পুলিশ।
এবার নিশ্চয়ই ফিরে আসবে নৌকোর লোকগুলো? মনে মনে আমরা সবাই চাইছিলাম ওরা ফিরে আসুক। কিন্তু তার বদলে যা হল সে একেবারে অপ্রত্যাশিত। হঠাৎ নৌকোর সব লোক এক সাথে গলা মিলিয়ে চিৎকার করতে শুরু করল : “আমরা কারা? বাস্তুহারা।”
জলের ওপর দিয়ে ভেসে আসা করুণ সেই চিৎকার শুনে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হল আমার। সেই মুহূর্তে মনে হল প্রতিবাদ নয়, এ যেন বিশ্বজগতের কাছে ওই মানুষগুলির ব্যাকুল জিজ্ঞাসা। যেন হতবুদ্ধি এই মানবজাতির হয়ে প্রশ্ন করছে ওরা। আমরা কারা? কোথায় আমাদের স্থান? সেই উচ্চারণ শুনতে শুনতে মনে হল ওরা তো আমারই হৃদয়ের গভীরতম অনিশ্চয়তার কথা বলছে–নদীর কাছে, স্রোতের কাছে। আমি কে? কোথায় আমার স্থান? কলকাতায় না এই ভাটির দেশে? ভারতে সীমান্তের ওপারে? গদ্যে না পদ্যে?
তারপর আমরা শুনতে পেলাম সে প্রশ্নের জবাব। নৌকো থেকে ভেসে এল কয়েকটা পুনরাবৃত্ত শব্দের একটা নতুন শ্লোগান : “মরিচঝাঁপি ছাড়ছি না, ছাড়ছি না, ছাড়ব না।”
ভটভটির ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলাম। অপূর্ব! যে জায়গা ছাড়তে প্রাণ চায় না সেই তো আমার দেশ।
ওদের চিৎকারে আমার ক্ষীণ কণ্ঠ মিলিয়ে আমিও বলে উঠলাম, “মরিচঝাঁপি ছাড়ব না!”
মোটরবোটের পুলিশগুলো উদ্বাস্তুদের ওই শ্লোগানের কী অর্থ করতে পারে সেটা ভাবার কথা আমার খেয়াল হয়নি। মিনিট কয়েক ধরে একই জায়গায় থেমে ছিল বোটটা; হঠাৎ দেখলাম ইঞ্জিন চালু করল। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে নৌকোটার থেকে দূরে সরে যেতে লাগল। খানিকক্ষণ পর্যন্ত মনে হল মন গলেছে পুলিশদের, উদ্বাস্তুদের ডিঙিটাকে ওরা চলে যেতে দেবে।
কিন্তু শিগগিরই ভুল ভাঙল। খানিকদূর যাওয়ার পর একটা চক্কর খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল বোটটা। তারপর হঠাৎ প্রচণ্ড গতিতে সোজা ছুটতে লাগল মানুষ আর মালপত্রে ভরা টলমলে নৌকোটার দিকে। ধাক্কাটা লাগল নৌকোর ঠিক মাঝখানটায়। চোখের সামনে কাঠের তক্তাগুলো টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে গেল চতুর্দিকে। জলের মধ্যে আঁকুপাকু করতে লাগল ডজন দুয়েক ছেলেবুড়ো মেয়েম।
হঠাৎ খেয়াল হল কুসুম আর ফকিরও তো থাকতে পারে ওদের মধ্যে। ধক করে উঠল আমার বুকের ভেতর।
আমরা চেঁচিয়ে আমাদের ভটভটিওয়ালাকে বললাম জায়গাটার আরেকটু কাছাকাছি যেতে–যদি একটু সাহায্য করতে পারি মানুষগুলোকে। ও একটু ইতস্তত করছিল, ভয় পাচ্ছিল যদি পুলিশ কিছু বলে। অনেক করে বোঝানো হল ভয়ের কোনও কারণ নেই, একদল স্কুলের মাস্টারমশাইকে পুলিশ কিচ্ছু বলবে না। অবশেষে রাজি হল ও।
আমরা এগোতে শুরু করলাম। খুব আস্তে আস্তে যেতে হচ্ছিল, পাছে জলের মধ্যে কারও সঙ্গে ধাক্কা লেগে যায়। ভটভটির ওপর থেকে হাত বাড়িয়ে দিলাম ভাসন্ত লোকগুলির দিকে। একজন দু’জন করে ডজনখানেক লোককে টেনে তোলা হল। ভাগ্যক্রমে জল খুব একটা গভীর ছিল না, অনেকেই তার মধ্যে পাড়ে গিয়ে উঠে পড়েছে।
ভটভটিতে টেনে তোলা একটা লোককে জিজ্ঞেস করলাম, “তুমি কুসুম মণ্ডলকে চেনো? ও কি ওই নৌকোয় ছিল?” দেখা গেল লোকটা চেনে কুসুমকে। মাথা নাড়ল ও। কুসুম মরিচঝাঁপিতেই আছে। প্রচণ্ড একটা স্বস্তিতে অবসন্ন হয়ে গেল শরীর। কিন্তু দ্বীপের ওপর ঘটনা যে কোন দিকে মোড় নিচ্ছে সে তখন আমি কিছুই জানি না।
এদিকে পুলিশের লোকগুলো তো তেড়ে এল আমাদের দিকে। ধমকে জিজ্ঞেস করল, “কে আপনারা? কী করছেন এখানে?”
আমাদের কোনও কথাতেই কান দিল না ওরা। বলল পুরো এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি আছে, বেআইনি জমায়েতের জন্য গ্রেফতার হয়ে যেতে পারি আমরা।
গুটিয়ে গেলাম আমরা। সবাই সাধারণ ইস্কুলমাস্টার, অনেকেরই বউ-বাচ্চা আছে; চুপচাপ পাড়ে গিয়ে জল থেকে টেনে তোলা মানুষগুলোকে নামিয়ে দিয়ে রওয়ানা হলাম ঘরের দিকে।
.
কলমের কালি ফুরিয়ে গেছে, পেন্সিলের টুকরোটার যেটুকু বাকি আছে এবার সেটা দিয়ে লিখছি। বাইরে পায়ের শব্দ শুনলেই মনে পড়ে যাচ্ছে যে-কোনও সময় কুসুম আর হরেন ফিরে আসবে, আর এসেই তক্ষুণি রওনা হয়ে পড়তে চাইবে হরেন। কিন্তু থামার উপায় নেই আমার। এখনও কত কী বলা বাকি রয়ে গেছে।
.
কথা
ছাদের ঘরের নিশ্চিন্ত আরামে বসে রাতের খাওয়ার কথা ভুলেই গিয়েছিল কানাই। কম্পাউন্ডের জেনারেটর থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আলোটা যখন নিভে গেল তখনও ও একমনে লেখাটা পড়ছে। আলো নিভতে মনে পড়ল ঘরের কোথাও একটা কেরোসিনের লক্ষ রয়েছে। অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে সেটা খুঁজছে কানাই, এমন সময় কার যেন পায়ের শব্দ পাওয়া গেল দরজার কাছে।
“কানাইবাবু?”
হাতে একটা মোমবাতি নিয়ে ময়না দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। “দেশলাই লাগবে?” জিজ্ঞেস করল কানাইকে। “আমি তো টিফিন ক্যারিয়ারটা নিয়ে যেতে এসেছিলাম। দেখলাম আপনি এখনও খাননি।”
“নীচেই যাচ্ছিলাম আমি,” বলল কানাই। “এ ঘরে কোথায় একটা হারিকেন ছিল না? খুঁজে পাচ্ছি না।”
“ওই তো ওখানে।”
মোমবাতি হাতে হারিকেনের কাছে গিয়ে কাঁচটা খুলে ফেলল ময়না। পলতেটা জ্বালাতে যেতেই হাত পিছলে গেল। মোমবাতি হারিকেন দুটোই ছিটকে পড়ল মাটিতে। চুরমার হয়ে গেল কাঁচটা আর কেরোসিনের কটু গন্ধে ভরে গেল সারা ঘর। মোমবাতিটা গড়াতে গড়াতে চলে গেল ঘরের এক কোণে। শিখা নিভে গেলেও সলতের ডগায় একটু লাল আভা তখনও দেখা যাচ্ছে। “জলদি!” মেঝের উপর উবু হয়ে বসে পড়ে মোমটার দিকে হাত বাড়াল কানাই। “পলতেটা টিপে নিভিয়ে দাও। নইলে কেরোসিনে আগুন ধরে সারা বাড়ি জ্বলে যাবে এক্ষুনি।”ময়নার হাত থেকে মোমবাতিটা নিয়ে বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মধ্যে টিপে নিজেই পলতেটা নিভিয়ে ফেলল কানাই। “যাক, নিভে গেছে। এবার কাঁচের টুকরোগুলো পরিষ্কার করতে হবে।”
“সে আমি করছি কানাইবাবু।”
“দু’জনে মিলে করলে তাড়াতাড়ি হবে।” ময়নার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে হাত দিয়ে সাবধানে মেঝেটা মুছতে লাগল কানাই।
“খাবারটা তো ঠান্ডা হয়ে গেল কানাইবাবু,” বলল ময়না। “খেয়ে নেননি কেন?”
“কালকের জন্যে তৈরি হচ্ছিলাম,” কানাই বলল। “ভোরবেলাতেই বেরিয়ে পড়তে হবে তো। আমিও যাচ্ছি, জানো কি?”
“জানি। মাসিমা বলেছেন। আপনি যাবেন শুনে আমি একটু খুশি হয়েছি।”
“কেন? আমার জন্যে খাবার আনতে আর ভাল লাগছে না?”
“না না,” বলল ময়না। “সে জন্যে নয়।”
“তা হলে?”
“আপনিও ওদের সঙ্গে যাবেন সেটা জেনেই অনেকটা শান্তি পেয়েছি। ওরা একা থাকবে না।”
“কারা?”
“ওরা দু’জন,” হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল ময়নার গলা।
“মানে ফকির আর পিয়া?”
“আর কে? যখন শুনলাম আপনি ওদের সঙ্গে যাবেন, এত নিশ্চিন্ত লাগল যে কী বলব। সত্যি কথা বলতে কী, আমি ভাবছিলাম যদি আপনি ওর সঙ্গে একটু কথা বলেন…”
“ফকিরের সঙ্গে? কী ব্যাপারে কথা বলব?”
“ওই যে, ওই মেমসাহেব মেয়েটার ব্যাপারে। আপনি যদি ওকে একটু বুঝিয়ে বলেন, মেয়েটা এখানে শুধু ক’দিনের জন্যে এসেছে, আবার ফিরে চলে যাবে…”
“কিন্তু সে কথা তো ফকির জানে। জানে না?”
অন্ধকারের মধ্যে শাড়ির খসখস শব্দ শোনা গেল। কাপড়টা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিল ময়না। “তাও, আপনার কাছ থেকে একবার শুনলে ভাল হবে, কানাইবাবু। কে জানে মনে মনে কী সব ভেবে বসে আছে ও। এত এত টাকা দিচ্ছে তো। ওই মেয়েটার সঙ্গেও যদি একটু কথা বলতে পারেন ভাল হয়। যদি একটু বুঝিয়ে বলেন, এরকমভাবে মাথা ঘুরিয়ে দিলে ফকিরের তাতে ভাল হবে না।”
“কিন্তু আমাকে কেন বলছ ময়না?” আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল কানাই। “আমি কী বলব বল?”
“কানাইবাবু, এখানে তো আপনিই শুধু ওদের দুজনের সঙ্গে কথা বলতে পারেন ফকিরের সঙ্গেও পারেন, আর ওই মেয়েটার সঙ্গেও পারেন। আপনিই তো ওদের দু’জনের মাঝখানে আছেন। আপনিই তো ওদের একজনের কথা শুনে আরেকজনকে বলবেন। আপনাকে ছাড়া ওদের কেউ তো জানতেই পারবে না অন্যজনের মনে কী আছে। এখন সবই আপনার হাতে কানাইবাবু। আপনি যা ইচ্ছে করবেন তাই বলাতে পারবেন ওদের মুখ দিয়ে।”
“আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না ময়না,” ভুরু কুঁচকে বলল কানাই। “কী বলতে চাইছ তুমি বলো তো? কীসের ভয় পাচ্ছ তুমি?”
“ও একটা মেয়ে, কানাইবাবু,” প্রায় ফিসফিস করে বলল ময়না। “আর ফকির একটা পুরুষ মানুষ৷”
অন্ধকারের মধ্যে ময়নার দিকে কটমট করে তাকিয়ে রইল কানাই। “আমিও তো একটা পুরুষ মানুষ, ময়না। তোমার কি মনে হয়, আমার কিংবা ফকিরের মধ্যে একজনকে যদি বেছে নিতে হয়, ও কাকে পছন্দ করবে?”
হ্যাঁ না কিছুই জবাব দিল না ময়না। ধীরে ধীরে বলল, “আমি কী করে বলব কানাইবাবু, কী আছে ওর মনে?”
ময়নার কথায় দ্বিধার সুরে একটু উত্তেজিত হয়ে উঠল কানাই। “আর তুমি? যদি সম্ভব হত তুমি কাকে বেছে নিতে আমাদের দু’জনের মধ্যে, ময়না?”
“কী বলছেন আপনি কানাইবাবু? ফকির আমার স্বামী,” শান্ত গলায় জবাব দিল ময়না। কিন্তু কানাই হাল ছাড়ার পাত্র নয়। “তুমি তো এত বুদ্ধিমতী মেয়ে ময়না, কত কী করতে পারো, ফকিরের কথা তুমি ভুলে যাও। তুমি বুঝতে পারছ না, ওর সঙ্গে থাকলে তুমি জীবনে কিছুই করে উঠতে পারবে না?”
“ও আমার ছেলের বাবা কানাইবাবু,” বলল ময়না। “আমি ওকে ছেড়ে যেতে পারি না। আমি যদি চলে যাই তা হলে ওর কী হবে?”
হাসল কানাই। “ঠিক আছে, ও তোমার স্বামী কিন্তু তা হলে তুমি নিজে কেন ওর সঙ্গে কথা বলতে পারছ না? এই কাজটা কেন তোমার হয়ে আমাকে করে দিতে হবে?”
“ও আমার স্বামী, সেইজন্যেই এই নিয়ে ওর সঙ্গে আমি কথা বলতে পারি না কানাইবাবু,” শান্তভাবে জবাব দিল ময়না। “একজন বাইরের লোকের সঙ্গেই শুধু এসব নিয়ে কথা বলা যায়।”
“তুমি নিজে যেটা করতে পারছ না সেটা একজন বাইরের লোক কী করে পারবে?”
“পারবে কানাইবাবু,” ময়না বলল। “কারণ মুখের কথা হল গিয়ে বাতাসের মতন। যখন হাওয়া দেয় তখন দেখবেন জলের ওপরে কেমন ঢেউ ওঠে৷ আসল নদীটা থাকে তার নীচে–তাকে দেখাও যায় না শোনাও যায় না। নদীর ভেতর থেকে কিন্তু হাওয়া দিয়ে ঢেউ তোলা যায় না। সেটা করা যায় বাইরে থেকে। সেটা করার জন্যেই আপনার মতো কাউকে আমার দরকার।”
আবার হেসে উঠল কানাই। “মুখের কথা বাতাসের মতো হতে পারে ময়না, কিন্তু সে কথার মারপ্যাঁচ তো দেখছি তোমার দিব্যি জানা আছে।”
উঠে পড়ে টেবিলটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল কানাই। “আচ্ছা, সত্যি করে বলো তো ময়না, তোমার কি কখনও মনে হয় না অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে যদি তুমি থাকতে তা হলে কেমন হত? কখনও কৌতূহল হয় না তোমার?”
একটা হালকা ঠাট্টার সুর ছিল কানাইয়ের কথাটার মধ্যে। ঠিক সেটাই দরকার ছিল ময়নাকে উশকে দেওয়ার জন্য। চটে উঠল ময়না। “আমাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছেন, তাই না কানাইবাবু? আপনি চান আমি একবার হা বলি, আর তাই নিয়ে আপনি মজা করবেন। সব লোককে বলে বেড়াবেন আমি এরকম বলেছি, তাই না? আমি গাঁয়ের মেয়ে হতে পারি, কিন্তু এত বোকা নই যে আপনার এই কথার জবাব দেব। যে মেয়ের সঙ্গেই আপনার দেখা হয় তার সঙ্গেই আপনি এই খেলা খেলেন–ঠিক বুঝতে পেরেছি আমি।”
ঠিক জায়গায় ঘা লাগল ময়নার এই শেষ কথাটায়। একটু যেন কুঁকড়ে গেল কানাই। তড়িঘড়ি বলল, “ময়না, শোনো, রাগ কোরো না–আমি খারাপ কিছু বলতে চাইনি।”
শাড়ির খসখস শব্দ শোনা গেল আবার। উঠে পড়ে এক টানে দরজাটা খুলে ফেলল ময়না। তারপর অন্ধকারের মধ্যেই কানাই শুনতে পেল ও বলছে, “ওই মেমসাহেবের সঙ্গে মনে হয় আপনার ভালই জমবে কানাইবাবু। সেটা হলেই আমাদের সকলের মঙ্গল।”
.
অপরাধ
বেশ কয়েকদিন ধরে চলল পুলিশি অবরোধ। পুরো ব্যাপারটাই আমাদের হাতের বাইরে, কিছুই করতে পারছি না, শুধু শুনতে পাচ্ছি নানারকম গুজব–কানে আসছে খুব সাবধানে খরচ করা সত্ত্বেও খাবার-দাবার সব শেষ হয়ে গেছে, খিদের জ্বালায় অনেকে নাকি ঘাস পর্যন্ত খাচ্ছে। সব টিউবওয়েলগুলো ভেঙে দিয়েছে পুলিশ, দ্বীপে কোনও খাওয়ার জল পাওয়া যাচ্ছে না। তেষ্টায় লোকে পুকুর-ডোবার জল খাচ্ছে, ফলে নাকি মারাত্মক কলেরা ছড়িয়ে পড়েছে মরিচঝাঁপিতে।
একদিন অবশেষে উদ্বাস্তুদের একজন পুলিশের চোখ এড়িয়ে পালিয়ে এল। সাঁতরে পার হয়ে গেল গারল নদী–নিঃসন্দেহে খুবই বীরত্বব্যঞ্জক কাজ। কিন্তু তাতেই সে থেমে থাকল না। বহু কষ্ট করে শেষে গিয়ে পৌঁছল কলকাতায়। সেখানকার সাংবাদিকদের সঙ্গে দেখা করে তাদের সমস্ত বৃত্তান্ত জানাল। পুরো ব্যাপারটা ফলাও করে ছাপা হল খবরের কাগজে। হুলুস্থুল পড়ে গেল চারদিকে। নাগরিক মঞ্চগুলি নানা জায়গায় আপিল করল, তুমুল হইচই হল বিধানসভায়, শেষে হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়াল ব্যাপারটা। আদালত রায় দিল এভাবে দ্বীপবাসীদের ঘেরাও করে রাখা বেআইনি, অবিলম্বে অবরোধ ওঠাতে হবে সরকারকে।
মনে হল একটা বড় জিত হল উদ্বাস্তুদের। খবরটা যেদিন আমাদের কাছে পৌঁছল, তার পরদিন দেখি বাঁধের কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে হরেন। মুখ ফুটে কিছু বলতে হল না–ঝোলা গুছিয়ে নিয়ে গুটিগুটি গিয়ে চেপে বসলাম ওর নৌকোয়। তারপর রওয়ানা দিলাম।
মনের মধ্যে তখন বেশ একটা ফুরফুরে ভাব। ভাবছি মরিচঝাঁপি গিয়ে নিশ্চয়ই দেখব মোচ্ছব চলছে, সকলে জয়ের আনন্দে মাতোয়ারা। কিন্তু পৌঁছে দেখি চিত্রটা একেবারেই অন্যরকম। এ কয়দিনের ঝড়ের আঘাতটা মারাত্মকভাবে লেগেছে মরিচঝাঁপিতে। তা ছাড়া অবরোধ উঠলেও পুলিশরা কিন্তু চলে যায়নি। এখনও তারা দ্বীপে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, সকলকে বলছে দ্বীপ ছেড়ে চলে যেতে।
কুসুমকে দেখে তো বুক ফেটে গেল আমার। শুকিয়ে কাঠির মতো হয়ে গেছে শরীর, চামড়া কুঁড়ে বেরিয়ে আসা হাড়গুলো যেন গোনা যায়। এত দুর্বল যে মাদুর ছেড়ে ওঠার ক্ষমতাটুকুও নেই। বরং ফকিরের ওপর দেখা গেল ততটা লাগেনি অবরোধের ধাক্কা–বাচ্চা বলেই হয়তো। ওই দেখাশোনা করছে মায়ের।
দেখেশুনে আমার মনে হল ফকির যাতে খেতে পায় সেইজন্য এই কয়দিন নিজে কিছু খায়নি কুসুম। কিন্তু দেখা গেল ব্যাপারটা অতটা সরল নয়। বেশিরভাগ সময়টাতেই কুসুম ফকিরকে ঘরে আটকে রাখার চেষ্টা করেছে, চারিদিকে থিকথিকে পুলিশের মধ্যে বাইরে যেতে দিতে চায়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও কঁক-ফোকর খুঁজে ফকির মাঝে মাঝেই বেরিয়ে গেছে, কখনও কয়েকটা কাঁকড়া, কখনও বা কিছু মাছ ধরে নিয়ে এসেছে। তার অধিকাংশটা কুসুম ওকেই খাইয়ে দিয়েছে। আর নিজে খেয়েছে একরকমের বুনো শাক–এখানকার লোকেরা তাকে বলে জাদু পালং। প্রথম প্রথম খেতে মন্দ লাগেনি। কিন্তু তারপর বোঝা গেল কী মারাত্মক ছিল সেই শাক। ভয়ানক পেটের গণ্ডগোল হল কুসুমের ওটা খেয়ে। একেই তো কয়েকদিন কোনও পুষ্টিকর খাবার পেটে পড়েনি, তার ওপর এই পেট খারাপ। সেইজন্যই এইরকম দশা দাঁড়িয়েছে কুসুমের।
ভাগ্যিস বুদ্ধি করে কিছু রসদ সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম আমরা খানিকটা চাল ডাল আর তেল। কুসুমের ঝুপড়ির মধ্যে এখন সেগুলি ঠিকমতো গুছিয়ে রাখতে লাগলাম। কিন্তু কুসুম সেসব কিছুই খাবে না। কোনওরকমে মাদুর থেকে উঠে একটা ব্যাগ টেনে তুলল নিজের কাঁধে, হরেন আর ফকিরকে বলল বাকিগুলো তুলে নিতে।
“আরে দাঁড়া দাঁড়া, কী করছিস তুই?” ভীষণ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি। “কোথায় যাচ্ছিস এগুলো নিয়ে? এ তো আমরা তোর জন্যে নিয়ে এসেছি।”
“আমি তো এগুলো রাখতে পারব না সার। এখন সব খাবার-দাবার খুব হিসেব করে খরচ করছি আমরা এখানে। এগুলো নিয়ে গিয়ে আমাদের পাড়ার নেতার কাছে জমা করতে হবে এক্ষুনি।”
যুক্তিটা আমি বুঝতে পারলাম। কিন্তু তাও অনেক করে বোঝালাম কুসুমকে–সবকিছু ভাগ করে খাওয়া হচ্ছে বলে যে সমস্তটাই উজাড় করে দিয়ে দিতে হবে তার কোনও মানে নেই। এর থেকে দু’-এক মুঠো চাল ডাল আলাদা করে রেখে দেওয়াটা কিছু অনৈতিক হবে না। বিশেষ করে ও যখন একটা বাচ্চার মা। তার দেখাশোনাও তো ওকে করতে হবে।
আমরা কাপে করে মেপে খানিকটা চাল ডাল তুলে রাখছি দেখে কাঁদতে শুরু করে দিল কুসুম। ওর সেই চোখের জল দেখে যেন একটা ঝাঁকুনি লাগল আমার আর হরেনের। এত ঝড়ঝঞ্জার মধ্যেও যে কুসুম সাহস আর মনোবল হারায়নি, তাকে এমন করে ভেঙে পড়তে দেখাটা বুকে শেল বেঁধার মতো যন্ত্রণাদায়ক। মায়ের পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দু’হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরল ফকির, আর পাশে বসে কুসুমের কাঁধে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল হরেন। আমি বসে রইলাম স্থাণু হয়ে। আমার তো কিছু দেওয়ার নেই এখানে, শুধু মুখের কথা ছাড়া।
“কী হল কুসুম?” জিজ্ঞেস করলাম আমি। “কী ভাবছিস রে?”
“কী জানেন সার,” আঁচলে চোখ মুছে বলল কুসুম, “খিদে-তেষ্টাটা তবু সহ্য হয়, কিন্তু তার চেয়েও বেশি কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে এই ক’দিনে। এই ঝুপড়ির মধ্যে অসহায়ভাবে বসে বসে শোনা–বাইরে পুলিশের দল দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, বারবার মাইকে বলছে আমাদের প্রাণের দাম এক কানাকড়িও নয়–সে যে কী ভয়ংকর সে আপনাকে কী বলব। বসে বসে খালি শুনেছি, এই দ্বীপকে রক্ষা করতে হবে গাছেদের জন্য, বন্য পশুদের জন্য। এই দ্বীপ ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সম্পত্তি, ব্যাঘ্র প্রকল্পের অংশ। সারা পৃথিবীর মানুষের পয়সায় এই প্রকল্প চলছে। প্রতিদিন খালি পেটে এখানে বসে বসে কতবার যে এই কথাগুলো শুনতে হয়েছে তার কোনও হিসেব নেই। মনে মনে ভেবেছি কারা এইসব লোক, যারা এত ভালবাসে বনের পশুদের যে তাদের জন্যে আমাদের মেরে ফেলতেও কোনও আপত্তি নেই? তারা কি জানে তাদের নাম করে কী করা হচ্ছে এখানে? কোথায় থাকে এই মানুষেরা? তাদের ঘরে কি ছেলেমেয়ে আছে? মা আছে? বাবা আছে? যত ভেবেছি তত মনে হয়েছে এই গোটা পৃথিবীটাই জন্তু জানোয়ারদের জায়গা হয়ে গেছে; আর আমাদের দোষ, আমাদের অপরাধ যে আমরা মানুষ হয়ে জন্মেছি, যেভাবে সবসময় মানুষ বাঁচার চেষ্টা করেছে, সেভাবে এই জল মাটির ওপর নির্ভর করে বাঁচতে চেয়েছি। সেই বাঁচার চেষ্টাকে যদি কেউ অপরাধ বলে মনে করে তা হলে সে ভুলে গেছে এভাবেই মানুষ বেঁচে এসেছে এতটা কাল মাছ ধরে, জঙ্গল সাফ করে আর সেই জমিতে চাষ করে।”
কথাগুলো শুনে আর ওর ভাঙাচোরা মুখটা দেখে এত খারাপ লাগল আমার–এই অকর্মণ্য সাধারণ ইস্কুল মাস্টারের–যে মাথাটা ঘুরতে শুরু করল হঠাৎ। মাদুরের ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়তে হল আমাকে।
.
বিদায় লুসিবাড়ি
গেস্ট হাউস থেকে বেরিয়ে হাসপাতালের রাস্তা ধরে কানাই যখন হাঁটতে শুরু করল লুসিবাড়ি তখন ভোরের কুয়াশায় ঢাকা। এই সাতসকালেও দেখা গেল একটা সাইকেল ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে গেটের সামনে। সেটাকে নিয়ে আবার গেস্ট হাউসে ফিরল কানাই। পিয়া আর ভ্যানওয়ালার সঙ্গে হাত লাগিয়ে মালপত্রগুলো তুলে ফেলল ভ্যানের পিছনে। মালপত্র বলতে খুব একটা বেশি কিছু না–কানাইয়ের সুটকেস, পিয়ার পিঠব্যাগ দুটো, আর গেস্ট হাউস থেকে ধার করা বালিশ কম্বলের একটা বান্ডিল।
বেশ জোরেই চলছিল ভ্যানটা। খানিকক্ষণের মধ্যেই গ্রামের সীমানায় এসে পড়ল ওরা। বাঁধের কাছাকাছি পৌঁছে হঠাৎ সামনের দিকে ইশারা করল ভ্যানওয়ালা। “ওই দেখুন, কী যেন একটা হচ্ছে ওখানে, ওই বাঁধের ওপরে।”
ভ্যানের তক্তার ওপর পা ঝুলিয়ে পেছন ফিরে বসেছিল কানাই আর পিয়া। ভ্যানওয়ালার কথা শুনে গলা বাড়িয়ে কানাই দেখল বাঁধের একেবারে ওপরে বেশ কিছু লোক জড়ো হয়েছে। মনে হল ওপারে কিছু একটা হচ্ছে কোনও প্রতিযোগিতা বা ওইরকম একটা কিছু। ভিড়ের সবাই মন দিয়ে দেখছে, কেউ কেউ মাঝে মাঝে চিৎকার করে উঠছে, মনে হল যেন উৎসাহ দিচ্ছে কাউকে। মালপত্র ভ্যানে রেখে কানাই আর পিয়াও উঠল বাঁধের ওপর, কী হচ্ছে দেখে আসতে।
ভাটা পড়ে গেছে। চড়াটার একেবারে শেষে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে মেঘা। পাশে ফকিরের ডিঙি। সেটাই দেখা গেল সম্মিলিত জনতার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। নৌকোর ওপর দাঁড়িয়ে ফকির আর টুটুল। তাদের পাশে হরেন আর তার সেই তেরো-চোদ্দো বছরের নাতি। একটা মাছধরা সুতোকে প্রাণপণে টেনে ধরে আছে ওরা। টানটান সুতোটা চিকচিক করছে আলো লেগে, তীব্র গতিতে জল কেটে এঁকেবেঁকে ছুটছে ডাইনে বাঁয়ে।
লোকজনকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল একটা শঙ্করমাছ গেঁথেছে ফকিরের বঁড়শিতে। কানাই আর পিয়ার চোখের সামনেই হঠাৎ ছাই রঙের চ্যাপটা জীবটা এরোপ্লেনের মতো ছিটকে উঠে এল জল থেকে। ফকিররা সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে গিয়ে ধরল সেটাকে। মনে হল যেন বিশাল একটা ঘুড়িকে টেনে নামিয়ে আনার চেষ্টা করছে। হাতে গামছা জড়িয়ে সর্বশক্তিতে মাছটাকে ধরে রেখেছে ওরা। আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে আসছে প্রাণীটার আছাড়ি পিছাড়ি। শেষ পর্যন্ত ডিঙির কিনার দিয়ে ঝুঁকে পড়ে দায়ের এক কোপে মাছটার ভবলীলা সাঙ্গ করল ফকির।
শিকার ডাঙায় এনে ফেলার পর ভিড় করে সেটাকে ঘিরে দাঁড়াল সবাই। পিয়া আর কানাইও গেল দেখতে। পাখনাগুলো মেলে ধরার পর দেখা গেল প্রায় মিটার দেড়েকের মতো চওড়া মাছটা। লেজের দৈর্ঘ্য মোটামুটি তার অর্ধেক। ওরা দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই একজন মাছওয়ালা দর দিল ওটাকে কেনার জন্য। রাজি হয়ে গেল ফকির। কিন্তু মাছটা নিয়ে যাওয়ার আগে দায়ের এক কোপে লেজটা কেটে নিয়ে ফকির টুটুলকে দিল সেটা। দেওয়ার ভঙ্গিটার মধ্যে এমন একটা আড়ম্বরের ভাব ছিল যে মনে হল যেন কোনও যুদ্ধ জয় করে আনা রত্নভাণ্ডার ছেলের হাতে তুলে দিচ্ছে ফকির।
“টুটুল ওটা দিয়ে কী করবে?” জিজ্ঞেস করল পিয়া।
“খেলবে-টেলবে আর কী,” জবাব দিল কানাই। “আগেকার দিনে রাজা জমিদাররা এই শঙ্করমাছের লেজের চাবুক দিয়ে অবাধ্য প্রজাদের শাসন করত। ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার। কিন্তু খেলনা হিসেবে জিনিসটা মন্দ নয়। আমারও একটা ছিল ছোটবেলায়।”
টুটুল তখনও মুগ্ধ হয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে লেজটাকে, এমন সময় ভিড় ঠেলে হঠাৎ ময়না এসে দাঁড়াল ওর সামনে। ঘাবড়ে গিয়ে একছুটে মায়ের নাগালের বাইরে পালাল টুটুল, গিয়ে লুকোল ফকিরের পেছনে। ছেলের গায়ে লেগে যাবে ভয়ে দু’হাতে রক্তমাখা দা-টা মাথার ওপরে তুলে ধরল ফকির। আর মায়ের হাত এড়িয়ে বাপের চারদিকে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল টুটুল। ভিড়ের সমস্ত লোক হো হো করে হেসে উঠল দৃশ্যটা দেখে।
ডিউটিতে যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়ে বেরিয়েছে ময়না। পরনে নার্সের পোশাক–নীল পাড় সাদা শাড়ি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টুটুলকে যখন ও ধরতে পারল, শাড়ি ততক্ষণে জলে কাদায় মাখামাখি। এত লোকের সামনে অপদস্থ হয়ে ঠোঁটদুটো অল্প অল্প কঁপছে ময়নার। ফকিরের দিকে ঘুরে তাকাল ও। চোখ নামিয়ে ফেলল ফকির। দা থেকে মুখের ওপর গড়িয়ে পড়া একটা রক্তের ফোঁটা মুছে নিল হাতের পেছনে।
“তোমাকে বলেছিলাম না ওকে সোজা স্কুলে নিয়ে যেতে?” ঝাঝালো গলায় বলল ময়না। “তুমি ওকে এখানে নিয়ে চলে এসেছ?”
ছেলের হাত থেকে শঙ্করমাছের লেজটা ছিনিয়ে নিল ও। বিষম খাওয়ার মতো একটা সম্মিলিত আওয়াজ উঠল ভিড় থেকে। একটানে লেজটাকে নদীর মধ্যে ছুঁড়ে দিল ময়না। মুহূর্তে স্রোতের টানে মিলিয়ে গেল ফকিরের বিজয়স্মারক। তারপর হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে চলল টুটুলকে। কান্নায় মুচড়ে গেল ছেলেটার মুখ। চোখদুটো চেপে বন্ধ করে চলতে লাগল মায়ের পেছন পেছন, যেন জোর করে দৃষ্টির আড়াল করে দিতে চাইছে চারপাশের সবকিছুকে।
কানাইয়ের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সামান্য কমে এল ময়নার চলার গতি। মুহূর্তের জন্য একবার চোখাচোখি হল দু’জনের। তারপর ছেলের হাত ধরে একদৌড়ে বাঁধের গা বেয়ে নেমে গেল ও। ময়না চোখের আড়ালে চলে যাওয়ার পর ফিরে তাকাল কানাই। দেখল ফকির একদৃষ্টে চেয়ে আছে ওর দিকে, মেপে নিচ্ছে ওকে। মনে হল কানাইয়ের সঙ্গে ময়নার নির্বাক ভাব বিনিময় নজরে পড়েছে ফকিরের–মনে মনে বোঝার চেষ্টা করছে তার মানেটা।
হঠাৎ খুব অস্বস্তি হতে লাগল কানাইয়ের। তাড়াতাড়ি পিয়ার দিকে ফিরে ও বলল, “চলুন, মালপত্রগুলো নামিয়ে ফেলি গিয়ে।”
.
ধকধক দমদম আওয়াজ তুলল ইঞ্জিন। ধীরে ধীরে লুসিবাড়ির চর ছেড়ে সরে যেতে লাগল মেঘা, আর ভটভটিটার পেছন পেছন দমকে দমকে এগোতে লাগল ফকিরের ডিঙি। মেঘার ইঞ্জিনের গতি বদলের সঙ্গে সঙ্গে এক-একবার টান পড়ছে ডিঙিতে বাঁধা দড়িতে, পরক্ষণেই আবার ঢিলে হয়ে যাচ্ছে। এই এলোমেলো গতিতে হঠাৎ ধাক্কা-টাক্কা যাতে না-লেগে যায়। সেজন্য ভটভটিতে না উঠে ডিঙিতেই রয়ে গেল ফকির। হাতে একটা লগি নিয়ে বসে রইল নৌকোর গলুইয়ে–ভটভটির খুব কাছে চলে এলে লগি দিয়ে ঠেলে সরিয়ে নিয়ে আসবে ডিঙিটাকে।
মেঘার ওপরের ডেকে সারেং-এর ঘরের পাশে দুটো উঁচু কাঠের চেয়ার রাখা, তারই একটায় গিয়ে বসেছিল কানাই। মাথার ওপর রোদ আড়াল করার জন্য একটা তেরপল টাঙানো। নির্মলের নোটবইটা কোলের ওপর খুলে রেখেছে কানাই, কিন্তু পড়ছে না। সার্ভের কাজের জন্য জিনিসপত্র গুছিয়ে তৈরি হচ্ছে পিয়া, তাকিয়ে তাকিয়ে তা-ই দেখছে ও।
গলুইয়ের সামনের দিকটা যেখানটায় একটু ছুঁচোলো হয়ে সামনে এগিয়ে গেছে, একেবারে তার কাছটায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল পিয়া। রোদ-হাওয়ার মুখোমুখি। ঠিকমতো দাঁড়িয়ে প্রথমে দূরবিনটা ঝুলিয়ে নিল গলায়, তারপর অন্য যন্ত্রপাতির বেল্টটা বাঁধতে লাগল। বেল্টের একদিকে লাগানো রয়েছে ক্লিপবোর্ড, আর অন্যদিকে ঝুলছে দু’খানা যন্ত্র–জিপিএস ট্র্যাকার আর ডেথ সাউন্ডার। বেল্ট-টেল্ট বাঁধা হয়ে গেলে তারপর দূরবিনটা তুলে নিয়ে চোখে লাগাল পিয়া। পা দুটো অনেকখানি ফাঁক করে দাঁড়িয়েছে, অল্প অল্প দুলছে ভটভটির দুলুনির সাথে সাথে। একমনে জলের দিকেই তাকিয়ে যদিও, কিন্তু কানাই বুঝতে পারছিল চারপাশে যা যা হচ্ছে–নৌকোর ওপরে কি নদীর পাড়ে–সবকিছুর প্রতিই বেশ সতর্ক রয়েছে পিয়া।
সূর্য যত ওপরে উঠতে লাগল ততই বাড়তে থাকল জলের ওপর থেকে ঠিকরে আসা আলোর তীব্রতা। বেলার দিকে একটা সময়ে সেই জোরালো বিচ্ছুরণে মুছে গেল জল আর আকাশের সীমারেখা। সানগ্লাস পরেও নদীর দিকে বেশিক্ষণ চোখ রাখা যায় না। পিয়া কিন্তু নির্বিকার। কী আলো, কী হাওয়া, কিছুতেই যেন কিছু আসে যায় না ওর। ভটভটির ঝাঁকুনি সামলানোর জন্য হাঁটুদুটো একটু ভাজ করে দাঁড়িয়ে কাজ করে যাচ্ছে একটানা, শরীরটা অল্প দুলছে পাশাপাশি, মনে হচ্ছে যেন খেয়ালই করছে না ঢেউয়ের দুলুনি। এতক্ষণে একটাই শুধু আপোশ করেছে–রোদ আড়াল-করা একটা টুপি বের করে পরে নিয়েছে মাথায়। তেরপলের আড়ালে বসে আলোর বিপরীতে ছায়ার মতো পিয়ার শরীরটা দেখতে পাচ্ছিল কানাই, চওড়া কানাওয়ালা টুপি আর যন্ত্রপাতি-ঝোলানো বেল্ট সমেত অনেকটা আমেরিকান কাউবয়দের মতো মনে হচ্ছিল ওর চেহারাটাকে।
বেলার দিকে হঠাৎ একবার একটু উত্তেজনার সঞ্চার হল বোটে। শোনা গেল ডিঙি থেকে চিৎকার করছে ফকির। ইশারায় হরেনকে ইঞ্জিন বন্ধ করতে বলে ডেকের পেছন দিকটায় দৌড় লাগাল পিয়া। কানাইও ছুটল পেছন পেছন, কিন্তু যতক্ষণে ও গিয়ে পৌঁছেছে তখন আর দেখার মতো কিছুই নেই।
“কী হল বলুন তো?”
একটা ডেটাশিটের ওপর ব্যস্ত হয়ে কীসব লিখে চলছিল পিয়া, মুখ তুলে তাকাল না। “ফকির একটা গ্যাঞ্জেটিক ডলফিন দেখতে পেয়েছে,” লিখতে লিখতেই জবাব দিল ও। “ভটভটির ডানদিকে, শ’ দুয়েক মিটার পেছনে। এখন আর চেষ্টা করে লাভ নেই, দেখতে পাবেন না। এতক্ষণে সাবধান হয়ে গেছে ওটা।”
পিয়ার গলায় সামান্য একটু হতাশা লেগে রয়েছে মনে হল কানাইয়ের। “এটাই কি প্রথম আজকে?”
“হ্যাঁ,” উৎসাহের সুরে জবাব দিল পিয়া। “এটাই প্রথম। তাতে অবশ্য আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। যা আওয়াজ।”
“ওরা কি ভটভটির শব্দে ভয় পেয়ে গেছে মনে হয়?”
“হতেই পারে,” পিয়া বলল। “আবার এরকমও হতে পারে যে আওয়াজটা মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত জলের নীচে ডুব দিয়ে থাকছে। যেমন ধরুন এই ডলফিনটা–আমরা ওটাকে পেরিয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে আসার পর জল থেকে মাথা তুলল ও।”
“আচ্ছা, আগে কি এখানে আরও বেশি ডলফিন দেখা যেত?”
“সে তো যেতই,” বলল পিয়া। “এইসব অঞ্চলের নদী-নালায় বিভিন্ন প্রজাতির জলজ স্তন্যপায়ী প্রাণী একসময় গিজগিজ করত। পুরনো তথ্য ঘাঁটলেই সে বিষয়ে নানা খোঁজখবর পাওয়া যায়।”
“তারা সব গেল কোথায়?”
“ব্যাপারটা কী জানেন, পরিবেশের পরিবর্তনের জন্যেই মনে হয় ডলফিনের সংখ্যা ক্রমশ কমে এসেছে এখানে। হয়তো আচমকা বড় রকমের কিছু একটা ঘটেছিল কোনও সময়।”
“তাই?” বলল কানাই। “আমার মেসোরও এইরকমই একটা ধারণা ছিল।”
“ধারণাটা ভুল ছিল না,” পিয়া একটু গম্ভীর। “একটা স্থায়ী বসবাসের জায়গা ছেড়ে যদি চলে যেতে শুরু করে এইরকম প্রাণীরা, বুঝতে হবে কোথাও খুব, খুব সাংঘাতিক কিছু একটা গোলমাল হয়েছে।”
“সে গোলমালটা কী হতে পারে বলে মনে হয় আপনার?”
“কোথা থেকে শুরু করি বলুন তো?” একটু শুকনো হেসে জিজ্ঞেস করল পিয়া। “বাদ দিন সেসব কথা। এই ইতিহাস ঘাঁটতে শুরু করলে চোখের জল সামলানো মুশকিল।”
খানিক পরে একটু জল খেয়ে নেওয়ার জন্যে পিয়া চোখ থেকে দূরবিনটা নামাতে কানাই বলল, “তো, আপনার কি তা হলে এটাই কাজ? এরকমভাবে সারাদিন জলের দিকে তাকিয়ে থাকা?”
কানাইয়ের পাশে এসে বসে পড়ল পিয়া। বোতল কাত করে খানিকটা জল গলায় ঢেলে বলল, “হ্যাঁ। সেটারও অবশ্য একটা পদ্ধতি আছে, কিন্তু বেসিক্যালি কাজটা তাই-ই। জলের দিকে তাকিয়ে থাকা। কিছু দেখতে পেলে ভাল, না পেলেও আফশোস খুব একটা নেই। সেটাও একটা তথ্য। সবটাই কাজে লাগে।”
না বোঝার ভাব করে মুখ বাঁকাল কানাই। বলল, “যার কাজ তাকে সাজে। আমি হলে তো পুরো একটা দিনও এই কাজ করে উঠতে পারতাম না। ভীষণ একঘেয়ে মনে হত।”
বোতলের জলটা শেষ করে ফেলল পিয়া। হাসল আবার। “সেটা আমি বুঝতে পারি। কিন্তু এই কাজের ধরনটাই তাই, জানেন? হয়তো অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করে বসে আছেন কিন্তু কিছুই ঘটছে না, আবার কখনও হয়তো সাংঘাতিক ব্যস্ততা। আর সে ব্যস্ততাটাও মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য। এই কাজের ছন্দটার সঙ্গে মানিয়ে নিতে খুব কম লোকই পারে। আমার তো মনে হয় দশ লাখে একটা পাওয়া যায় সেরকম লোক। সে কারণেই এখানে ফকিরের মতো একটা লোককে পেয়ে খুব আশ্চর্য হয়েছি আমি।”
“আশ্চর্য হয়েছেন? কেন?”
“ডলফিনটাকে কেমন স্পট করল ও দেখলেন তো?” বলল পিয়া। “যেন সব সময়ই জলের দিকে নজর রেখে চলেছে ও। নিজের অজান্তেই। এর আগেও অনেক অভিজ্ঞ জেলের সঙ্গে কাজ করেছি আমি, কিন্তু এরকম অদ্ভুত ইন্সটিংক্ট আমি কারওর মধ্যে দেখিনি। নদীর বুকের ভেতরটা পর্যন্ত যেন দেখে নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে ওর।”
পিয়ার কথাটা হজম করতে এক মুহূর্ত সময় লাগল কানাইয়ের। “তা হলে ওর সঙ্গেই কাজ চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে আপনার?”
“ওর সঙ্গে আবার কাজ করার ইচ্ছে তো আমার আছে বটেই,” বলল পিয়া। “আমার মনে হয় ফকিরের সঙ্গে মিলে কাজ করতে পারলে অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারা যাবে।”
“মনে হচ্ছে আপনার কিছু একটা লং-টার্ম প্ল্যান রয়েছে?” মাথা নাড়ল পিয়া। “সত্যি বলতে কী, সেরকম ইচ্ছে একটা আছে। একটা প্রজেক্টের কথা আমার মাথায় ঘুরছে, সেটা যদি হয় তা হলে বেশ কয়েক বছরই হয়তো এখানে থেকে যেতে হবে আমাকে।”
“এখানে? মানে এই সুন্দরবনে?”
“হ্যাঁ।”
“সত্যি?” কানাইয়ের ধারণা ছিল সামান্য কয়েকদিনের জন্যেই ইন্ডিয়ায় এসেছে পিয়া। কিন্তু ও যে এদেশে বেশ কিছুদিন থেকে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে তাও কোনও শহর-টহরে নয়, সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও এই ভাটির দেশের জলকাদার মধ্যে সেটা জানতে পেরে বেশ একটু অবাকই হয়ে গেল কানাই।
“আপনি ভাল করে ভেবে নিয়েছেন তো? এইরকম একটা জায়গায় থাকতে পারবেন আপনি বছরের পর বছর?” ও জিজ্ঞেস করল।
“কেন পারব না?”কানাইয়ের প্রশ্নটা শুনে একটু অবাকই হল পিয়া। “না পারার তো কিছু নেই।”
“আর এখানে থাকলে এই ফকিরের সঙ্গেই কাজ করবেন?”
মাথা নাড়ল পিয়া। “খুবই খুশি হব যদি তা সম্ভব হয়। কিন্তু সেটা আমার মনে হয় ফকিরের ওপরই নির্ভর করছে।”
“অন্য আর কেউ কি আছে যার সঙ্গে আপনি কাজটা করতে পারেন?”
“সেটা এক ব্যাপার হবে না কানাই,” পিয়া বলল। “ফকিরের পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা অসাধারণ। সকলের এরকম থাকে না। গত ক’দিন ওর সঙ্গে কাজ করতে যে কী ভাল লেগেছে সেটা আমি আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। এত সুন্দর রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা আমার খুব কমই হয়েছে।”
কানাইয়ের মনের ভেতরে কোথায় হঠাৎ একটা ঈর্ষার তীক্ষ্ণ খোঁচা লাগল। নিজেকে সামলাতে না-পেরে একটু ব্যঙ্গের সুরে বলল, “আর এই পুরো সময়টায় ও যা যা বলেছে তার একটা বর্ণও আপনি বুঝতে পারেননি। ঠিক বলছি?”
“পারিনি,” সম্মতিতে মাথা নাড়ল পিয়া। “কিন্তু মজার ব্যাপারটা কী জানেন? আমাদের দু’জনের মধ্যে এত বিষয়ে মিল যে ভাষার ব্যবধানটার জন্য অসুবিধাই হয়নি কোনও।”
“শুনুন পিয়া,” স্পষ্ট গলায় খানিকটা কর্কশভাবে বলল কানাই। “নিজের সঙ্গে ছলনা করার চেষ্টা করবেন না। ফকির আর আপনার মধ্যে কোনও মিল কোনওকালে ছিল না, এখনও নেই। ফকির একটা জেলে, আর আপনি একজন সায়েন্টিস্ট। যে জীবজগৎ আপনার কাছে গবেষণার বিষয়, ওর চোখে সেটা খাবার জিনিস। জীবনে কখনও চেয়ারে বসেনি ও, আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি। কল্পনা করতে পারেন প্লেনে চড়লে ওর কী অবস্থা হবে?” জেটপ্লেনের সারি সারি চেয়ারের মধ্যে দিয়ে লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরে ফকির হেঁটে যাচ্ছে দৃশ্যটা কল্পনা করেই হেসে ফেলল কানাই। “আপনাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র কোনও মিল নেই পিয়া। থাকতে পারে না। আপনারা দুজনে দুটো আলাদা দুনিয়ার মানুষ, আলাদা জগতের। আপনার ওপর বজ্রাঘাত হতে যাচ্ছে বুঝতে পারলেও আপনাকে সেটা জানানোর কোনও উপায় নেই ফকিরের হাতে।”
ঠিক তক্ষুনি, কানাইয়ের কথার সূত্র ধরেই যেন, হঠাৎ ফকিরের চিৎকার শোনা গেল– ভটভটির ইঞ্জিনের শব্দের ওপর গলা চড়িয়ে চেঁচিয়ে বলছে, “কুমির! কুমির!”
“কী বলল ওটা?” ডেকের পেছনদিকে দৌড়ে গেল পিয়া। কানাইও দৌড়াল ওর সঙ্গে সঙ্গে।
ডিঙির ওপর ছইয়ের গায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে নদীর ভাটির দিকে ইশারা করছে ফকির। “কুমির!”
“কী দেখতে পেয়েছে ও?” দূরবিন তুলে চোখে লাগাল পিয়া।
“আ ক্রোকোডাইল।”
এরকম একটা তাৎক্ষণিক উদাহরণ হাতের সামনে পেয়ে সেটা ব্যবহার করার সুযোগটা আর ছাড়তে পারল না কানাই। “আপনি নিজেই দেখুন পিয়া, যদি আমি এখন এখানে না থাকতাম আপনি বুঝতেই পারতেন না কী দেখে চেঁচিয়ে উঠল ফকির।”
দূরবিনটা চোখ থেকে নামিয়ে বোটের সামনে ফিরে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াল পিয়া। ঠান্ডা গলায় বলল, “আপনার বক্তব্য আমি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি কানাই। থ্যাঙ্ক ইউ।”
“শুনুন,” পিছু ডাকল কানাই। “পিয়া–” কিন্তু দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে। পিয়া ফিরে গেছে নিজের জায়গায়। মাফ চাওয়ার জন্য ঠোঁটের ডগায় আসা শব্দগুলি গিলে নিতে হল কানাইকে।
মিনিট কয়েক পর কানাই দেখল বোটের সামনের দিকটায় ফের গিয়ে দাঁড়িয়েছে পিয়া, চোখের সঙ্গে সাঁটা দূরবিন, এমন মগ্ন হয়ে তাকিয়ে আছে জলের দিকে যে কানাইয়ের মনে হল ও যেন পুঁথিপড়া পণ্ডিত–কোনও পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার করার চেষ্টা করে যাচ্ছে গভীর মনোযোগে। পৃথিবী যেন নিজের হাতে লিখে রেখেছে দুপাঠ্য সেই পুঁথি। দেখতে দেখতে কানাইয়ের মনে পড়ল ও নিজে প্রায় ভুলেই গেছে কেমন লাগে কোনও কিছুর দিকে এভাবে নিবিষ্ট হয়ে তাকিয়ে থাকতে। কোনও ভোগ্যদ্রব্য নয়, সুখসুবিধার উপকরণ নয়, লালসা নিবৃত্তির বস্তু নয়–এরকম আপাত-অর্থহীন কিছুর দিকে এমন নিমগ্ন হয়ে চেয়ে থাকা আর হয় না এখন। অথচ একটা সময় ছিল যখন ও-ও পারত এইভাবে মনটাকে একটা বিন্দুতে নিয়ে আসতে; ঠিক এইরকম একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকত অজানার দিকে–যেন একটা চশমার ভেতর দিয়ে। কিন্তু ওর সেই দৃশ্যবস্তু লুকোনো থাকত বিভিন্ন বিজাতীয় ভাষার গভীরে। ভাষার সেই দিগন্তছোঁয়া প্রান্তরে পৌঁছে অদ্ভুত একটা তৃষ্ণার বোধ জাগত মনে, ঠিক কোন পথ দিয়ে এসে অন্য বাস্তবেরা এক জায়গায় মিলে যায় খুঁজে বের করার ইচ্ছে হত সেটা। সে যাত্রার পথের বাধাগুলির কথাও এখন স্পষ্ট মনে পড়ল কানাইয়ের–সেই হতাশার কথা, যখন এক এক সময় মনে হত কিছুতেই ওই শব্দগুলিকে ঠিকমতো তুলে আনা যাবে না ঠোঁটে, ঠিক ঠিক ওই আওয়াজগুলো মুখ দিয়ে বের করতে পারা যাবে না কোনওদিন, যেমন দরকার ঠিক সেভাবে বাক্য জুড়ে জুড়ে কথা বলা আর হয়ে উঠবে না, চেনা ছক ভেঙে গুঁড়িয়ে আবার নতুন করে শুরু করতে হবে সবকিছু। শুধুমাত্র একটা উদগ্র ইচ্ছায় তখন দ্রুতগতি হয়ে উঠত মন, আর সে উত্তেজনা মনে মনে এখনও অনুভব করছে কানাই। কাম্য বস্তুর চেহারাটা কেবল পালটে গেছে, সেই তীব্র বাসনা এখন জলজ্যান্ত একটা মেয়ের চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওর সামনে, এই বোটের ওপর রক্তমাংসে গড়া সেই ভাষার শরীর।
.
ব্যাঘাত
লুসিবাড়ি ছাড়ার পর থেকেই নির্মলের নোটবইটা নিয়ে হরেনের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ খুঁজছিল কানাই। বেশ খানিকক্ষণ পর মেঘা যখন অবশেষে একটা খোলা জায়গায় এসে পড়ল, তখন ও আস্তে আস্তে উঠে সারেঙের ঘরটায় গিয়ে ঢুকল। নোটবইটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, “এটা চিনতে পারেন হরেনদা?”
সামনে জলের দিকে চেয়েছিল হরেন। মুহূর্তের জন্য একবার নজর ফিরিয়ে দেখল নোটবইটা। নিরুত্তাপ গলায় বলল, “হ্যাঁ। সার ওটা আমাকে রাখতে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন আপনাকে দিয়ে দিতে।”
হরেনের সংক্ষিপ্ত জবাবে একটু চুপসে গেল কানাই। নির্মলের লেখায় বিভিন্ন প্রসঙ্গে এতবার হরেনের উল্লেখ আছে যে কানাই ভেবেছিল নোটবইটা দেখে ঠিক আবেগের বন্যায় ভেসে না গেলেও দু-একটা পুরনো স্মৃতি নিশ্চয়ই উশকে উঠবে ওর মনে।
“মেসো আপনার কথা অনেক লিখেছে এর মধ্যে,” ওকে একটু উৎসাহিত করার জন্য বলল কানাই। হরেন কিন্তু চোখই সরাল না জল থেকে। মাথাটা অল্প একটু নাড়াল শুধু।
ওর পেট থেকে কিছু বের করা খুব একটা সহজ কাজ হবে না বুঝতে পারল কানাই। এতটাই কি কম কথা বলে ও? নাকি বাইরের লোকের সামনে মুখ খুলতে চাইছে না? বলা মুশকিল।
“কোথায় ছিল খাতাটা?” কানাই নাছোড়বান্দা। “কোত্থেকে বেরোল এতদিন পরে?”
গলাটা একটু সাফ করে নিল হরেন। বলল, “হারিয়ে গিয়েছিল।”
“কী করে?”
“আপনি জানতে চাইলেন তাই বলছি,” বলল হরেন। “সার খাতাটা আমাকে দেবার পর আমি ওটাকে বাড়ি নিয়ে গেলাম। তারপর জল-টল যাতে না লাগে সেজন্য ভাল করে । প্লাস্টিকে মুড়ে আঠা লাগিয়ে আঠাটা শুকোনোর জন্যে রোদে দিলাম। তো বাড়ির কোনও বাচ্চা (ফকির কি?) ওটাকে খেলার জিনিস ভেবে উঠিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছিল। তারপর বাচ্চাদের যেমন স্বভাব–বেড়ার খাঁজের মধ্যে ওটাকে লুকিয়ে রেখে ভুলেই গেল সে কথা। আমি চারদিকে কত খুঁজলাম, কিছুতেই পেলাম না। তারপর আস্তে আস্তে আমিও একসময় ভুলে গেলাম খাতাটার কথা।”
“শেষপর্যন্ত কী করে পাওয়া গেল তারপর?”
“বলছি সে কথা,” শান্ত, মাপা গলায় বলতে লাগল হরেন। “প্রায় বছর খানেক হবে–আমি ঠিক করলাম আমাদের পুরনো চালাঘরটা ভেঙে একটা পাকা বাড়ি বানাব। সেই ঘর ভাঙার সময়ই খুঁজে পাওয়া গেল ওটা। আমাকে যখন এনে দিল খাতাটা আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না কী করব ওটাকে নিয়ে। ডাকে পাঠাতে চাইনি, যদি ঠিকানা ভুল হয়ে যায়। আর মাসিমাকে নিয়ে গিয়ে যে দেব, সে সাহসও আমার ছিল না। কত বছর হল ওনার সঙ্গে কোনও কথাই হয়নি। তারপর খেয়াল হল ময়না তো যায় মাঝে মাঝে গেস্ট হাউসে। শেষে ওর হাত দিয়েই পাঠিয়ে দিলাম খাতাটা। ওকে বললাম, “এটা নিয়ে চুপচাপ সারের পুরনো পড়ার ঘরটাতে গিয়ে রেখে দিয়ে আয়। সময় হলে ওরা ঠিক খুঁজে পাবে। তো এই হল ঘটনা।”
এই বলে মুখ বন্ধ করল হরেন। এমনভাবে কথাটা শেষ করল যে বোঝা গেল এই বিষয়ে আর কোনও বাক্যব্যয় করতে রাজি নয় ও।
.
ঘণ্টা তিনেক একটানা চলার পর হঠাৎ একবার ইঞ্জিনের শব্দটা মুহূর্তের জন্য বেতালা শোনাল পিয়ার কানে। মেঘার ডেকের ওপর একইভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ও, কিন্তু শুরুতে সেই যে একটা গ্যাঞ্জেটিক ডলফিনকে একঝলক দেখা গিয়েছিল, তারপর থেকে এ পর্যন্ত কিছুই আর চোখে পড়েনি। তার ফলে ওর সেই দহটাতে তাড়াতাড়ি গিয়ে পৌঁছনোর ইচ্ছেটা আরও বেড়েছে বই কমেনি৷ এইসময় যদি ইঞ্জিন গড়বড় করে তা হলে খুবই আফশোসের ব্যাপার হবে। জলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই কান খাড়া করে ইঞ্জিনের আওয়াজটা শুনতে লাগল পিয়া। খানিকক্ষণের মধ্যেই ধকধক শব্দের ছন্দটা আবার ফিরে আসতে হাঁফ ছাড়ল ও।
কিন্তু বেশিক্ষণের জন্য নয়। মিনিট পনেরো পরেই ফের তাল কাটল ইঞ্জিনের। একটা ফঁপা ফটফট আওয়াজ হল কয়েকবার, তারপর ক্লান্ত কাশির মতো কয়েকটা শব্দ, তারপর আচমকা সব চুপচাপ। মোহনার মাঝ বরাবর এসে একেবারে থেমে গেল মেঘার ইঞ্জিন।
পিয়া বুঝতে পারছিল এ গোলমাল সহজে সারবার নয়। এত বিরক্ত লাগছিল যে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতেও ইচ্ছে করছিল না। কেউ না কেউ এক্ষুনি সেটা জানাতে আসবে নিশ্চয়ই, তাই ইঞ্জিনঘরের দিকে এগিয়ে দেখার চেষ্টা না করে নিজের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রইল ও। বাতাসে ঢেউ তোলা নদীর দিকে চেয়ে দেখতে লাগল এক মনে।
যা ভাবা গিয়েছিল, খানিক বাদেই গুটিগুটি পায়ে কানাই এসে দাঁড়াল পাশে। “একটা খারাপ খবর আছে পিয়া।”
“আজকে আর হবে না, তাই তো?”
“মনে হয় না।”
হাত তুলে দূরে পাড়ের দিকে ইশারা করল কানাই। ওখানে একটা ছোট গ্রাম আছে। স্রোতের টানে টানে ওই পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়াটা নাকি খুব একটা সমস্যা হবে না, হরেন বলেছে। সেখানে হরেনের কিছু আত্মীয়স্বজন আছে। তাদের একজন নাকি এইসব ইঞ্জিন-টিঞ্জিনের কাজ জানে। সব যদি ঠিকঠাক চলে তা হলে কাল সকাল নাগাদ গর্জনতলার দিকে রওয়ানা হওয়া যেতেও পারে।
পিয়া মুখ বাঁকাল। “কী আর বলব? কী আর করা যাবে এ ছাড়া।”
“নাঃ। সত্যিই আর কোনও উপায় নেই।”
ইতোমধ্যে ভটভটিটাকে ঘুরিয়ে নিয়েছে হরেন। বোটের মুখ এখন দূরের ওই গাঁয়ের দিকে। খানিকক্ষণের মধ্যেই বোঝা গেল স্রোতের টানে ধীরে ধীরে মোহনা পেরিয়ে যাচ্ছে ওরা। যদিও ভাটা পড়ে গেছে, ফলে নদীর টান এখন ওদের অনুকূলে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভয়ানক আস্তে আস্তে এগোচ্ছে মেঘা। অবশেষে যখন গন্তব্য স্পষ্টভাবে নজরে এল, দিন তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।
দেখা গেল মোহনার ঠিক ধারে নয় গ্রামটা। একটু ভেতরে, কয়েক কিলোমিটার চওড়া একটা নদীর পাড়ে। ভাটা চলছে বলে এখন পাড়টাকে মনে হচ্ছে আকাশছোঁয়া, বোট থেকে। গ্রামটা চোখেই পড়ছে না। বাঁধের মাথায় শুধু দেখা যাচ্ছে বেশ কয়েকটা জটলা–কিছু লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেন অপেক্ষা করছে মেঘার জন্য। ভটভটিটা কাছাকাছি পৌঁছতে দেখা গেল কয়েকজন নেমে আসছে কাদা ভেঙে, হাত নাড়ছে ওদের উদ্দেশে। জবাবে বোটের রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে হাত দুটো মুখের সামনে জড়ো করে এক হাঁক পাড়ল হরেন। খানিক বাদেই দেখা গেল একটা নৌকো সড়সড় করে পাড় বেয়ে নেমে জলে পড়ল, তারপর আস্তে আস্তে এসে থামল মেঘার পাশে। দুটো লোক ছিল নৌকোটায়। একজনকে আলাপ করিয়ে দিল হরেনের আত্মীয় বলে, সামনের গ্রামটাতেই সে থাকে, পেশায় জেলে। আর অন্যজন তার বন্ধু, পার্ট-টাইম মোটর মিস্ত্রি। বেশ খানিকক্ষণ ধরে চলল আলাপ পরিচয়ের পালা, তারপর ওদের দুজনকে নিয়ে হরেন নেমে গেল ভটভটির খোলের ভেতর। কিছুক্ষণের মধ্যেই মিস্ত্রির যন্ত্রপাতির আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ল গোটা বোটে। হাতুড়ি-বাটালির প্রবল খটখট শব্দের মধ্যে অস্ত গেল সূর্য।
খানিক পরে সন্ধের আবছায়া চিরে হঠাৎ বিকট একটা জান্তব আওয়াজ শোনা গেল; মনে হল প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে কাতর আর্তনাদ করছে কেউ। হাতে টর্চ নিয়ে পিয়া আর কানাই দৌড়ে বেরিয়ে এল নিজের নিজের কেবিন থেকে। দু’জনেরই মাথায় একই চিন্তা। কাউকে নিশ্চয়ই বাঘে ধরেছে, তাই না?” জিজ্ঞেস করল পিয়া।
“জানি না।”
রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে চেঁচিয়ে হরেনকে কী একটা জিজ্ঞেস করল কানাই। এক মুহূর্তের জন্য থেমে গেল হাতুড়ির আওয়াজ। তারপরেই খোলের ভেতর থেকে ভেসে এল। হরেনদের অট্টহাসির শব্দ।
“ব্যাপারটা কী?” পিয়া কানাইয়ের দিকে তাকাল।
কানাইয়ের মুখেও হাসি। বলল, “আমি জিজ্ঞেস করলাম কাউকে বাঘে ধরেছে কিনা, তাতে ওরা বলল গাঁয়ে একটা মোষ বাছুর বিয়োচ্ছে, ওটা তারই আওয়াজ।”
“কী করে জানল ওরা?”
“কারণ মোষটার মালিক হরেনের আত্মীয়। বাঁধের একেবারে পাশেই ওদের বাড়ি–ওই দিকটায়।”
পিয়াও হেসে ফেলল এবার। “আমরা মনে হয় খামখাই ঘাবড়ে যাচ্ছি।” দু’ হাতের আঙুলগুলো জড়ো করে লম্বা একটা আড়মোড়া ভাঙল ও। হাই তুলল একবার। “সকাল সকাল শুয়ে পড়তে হবে মনে হচ্ছে।”
“আজকেও?” একটু বিরক্তির আভাস কানাইয়ের গলায়। তারপর, যেন বিরক্ত ভাবটাকে চাপা দেওয়ার জন্যই যোগ করল, “খাওয়া-দাওয়া করবেন না?”
“একটা নিউট্রিশন বার খেয়ে নেব। তাতেই কাল সকাল পর্যন্ত চলে যাবে আমার। কিন্তু আপনার কী প্ল্যান? অনেক রাত পর্যন্ত জাগবেন নাকি?”
“হ্যাঁ, কানাই বলল। “মনুষ্যজগতের অধিকাংশের মতো এই অধমেরও নিশাকালে কিঞ্চিৎ আহার্য গ্রহণের বদভ্যাস আছে। আর, আজকে তারপরেও খানিকক্ষণ জেগে থাকার পরিকল্পনা আছে আমার–মেসোর নোটবইটা আজকেই পড়ে শেষ করব ঠিক করেছি।”
“পড়া কি প্রায় হয়ে এসেছে?”
“হ্যাঁ, শেষের দিকে,” বলল কানাই।
.
বাঁচা
লুসিবাড়িতে যখন পৌঁছলাম তখনও আমার শরীর বেশ খারাপ। নীলিমা হরেনকে বকাবকি করতে লাগল। বলল, “তোমার জন্যেই এরকম হল। কেন বারবার ওকে টেনে নিয়ে যাও মরিচঝাঁপিতে? দেখো তো এখন, কীরকম অসুস্থ হয়ে পড়ল মানুষটা।”
সুস্থ যে আমি ছিলাম না সে কথা ঠিক–নানারকম স্বপ্ন, কল্পনা আর ভয়ের চিন্তায় সবসময় ভরে থাকত মাথাটা। এমনও অনেকদিন হয়েছে যে বিছানার থেকে ওঠারই ক্ষমতা হয়নি–চুপচাপ শুধু শুয়ে থেকেছি আর রিলকের কবিতা পড়েছি, ইংরেজিতে আর বাংলায়।
আমার সঙ্গে অনেক নরম সুরে কথা বলত নীলিমা তখন। “কতবার বলিনি তোমাকে ওখানে না যেতে? বলো? বলিনি এইরকম অবস্থা দাঁড়াবে একদিন? তুমি যদি সত্যি সত্যি কিছু করতে চাও তা হলে তো ট্রাস্টের কাজেই সাহায্য করতে পারো। হাসপাতালটার জন্যে কিছু কিছু কাজ করতে পারো। তার জন্য মরিচঝাঁপিতে কেন যেতে হবে?”
“সে তুমি বুঝবে না নীলিমা।”
“কেন নির্মল? বলো আমাকে। কিছু কিছু গুজব আমার কানে এসেছে। সবাই নানারকম কানাঘুষো করছে। কুসুমের সঙ্গে কি এসবের কোনও সম্পর্ক আছে?”
“এটা তুমি কী বললে নীলিমা? এতগুলি বছর তো আমার সঙ্গে কাটালে–কখনও কি এ ধরনের কোনও চিন্তার কোনও কারণ ঘটেছে?”
নীলিমা কাঁদতে শুরু করল। “লোকে তো সেসব কথা বুঝবে না নির্মল। চারদিকে কুৎসিত গুজব রটছে, কান পাতা যায় না।”
“নীলিমা, এ সমস্ত গুজবে কান দেওয়া কি তোমাকে মানায়, বলো?”
“তা হলে কুসুমকে এখানে নিয়ে এসো। ও এখানে থেকে ট্রাস্টের কাজ করুক। তুমিও করো।”
কী করে ওকে বোঝাব আমি, যে ট্রাস্টের কাজ করার জন্য আমার থেকে ভাল লোক অনেক আছে। আমি তো এখানে শুধু কলম পেষার কাজ করতে পারব, যন্ত্রের মতো, দম দেওয়া খেলনার মতো। কিন্তু মরিচঝাঁপির ব্যাপারটা আলাদা। রিলকে আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন কী করতে পারি আমি ওখানে। আমারই জন্য একটা কবিতায় গোপন সংকেত রেখে গেছেন কবি–শুধু আমার জন্য। সে সংকেতের লুকোনো অর্থ খুঁজে বের করেছি আমি। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। শুধু সেই ব্রাহ্মমুহূর্তের জন্য বসে আছি আমি, অপেক্ষা করে আছি একটা ইশারার জন্য। সে ইশারা পেলে কী করব সেটা আর বলে দিতে হবে না।
কারণ, কবি নিজেই আমাকে বলে গেছেন–
‘এখানেই উচ্চার্যের মাতৃভূমি। এই তার কাল।
বল, তা ঘোষণা কর…’
দিনের পর দিন চলে গেল, সপ্তাহের পর সপ্তাহ–অবশেষে শরীরে বল ফিরে পেতে লাগলাম আমি, মনে হল আস্তে আস্তে আবার গিয়ে বসা যেতে পারে পড়ার ঘরটাতে। প্রতিদিন সকাল আর দুপুরগুলো কাটাতে লাগলাম ওখানে বিস্তীর্ণ শূন্য সেই সময়প্রান্তর পার করতাম মোহনার দিকে তাকিয়ে, বসে বসে চেয়ে দেখতাম কেমন করে আস্তে আস্তে জল নামছে, খালি হচ্ছে মোহনা, ফের ভরে যাচ্ছে, ফের খালি হচ্ছে, ফের ভরে যাচ্ছে, দিনের পর দিন, পৃথিবীর মতো ক্লান্তিহীন।
একদিন দুপুরে, দ্বিপ্রহরিক বিশ্রামের পর অন্যান্য দিনের তুলনায় খানিকটা আগেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছি নীচে, এমন সময় নীলিমার গলা কানে এল। গেস্ট হাউসে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে, গলার স্বরে বুঝতে পারলাম কে, আগের দিন রাতে ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা হয়েছিল আমার। লোকটি কলকাতার ডাক্তার, সাইকিয়াট্রিস্ট। নীলিমা বলছিল খুব ভয় পাচ্ছে ও, খুবই চিন্তায় আছে আমাকে নিয়ে। ও এমন একটা খবর জানতে পেরেছে যেটা শুনলে আমি নাকি অস্থির হয়ে পড়ব, কী করে সেটা আমার থেকে গোপন রাখা যায় সে বিষয়ে ডাক্তারবাবুর পরামর্শ চাইছিল।
“খবরটা কী?” জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার।
“আপনার হয়তো ব্যাপারটা সেরকম সাংঘাতিক কিছু মনে হবে না,” বলল নীলিমা। “এখান থেকে কিছু দূরে একটা দ্বীপ আছে–মরিচঝাঁপি বলে–সেইটার দখল নিয়ে গণ্ডগোল। একদল বাংলাদেশি উদ্বাস্তু ওই দ্বীপটায় এসে উঠেছে, আর কিছুতেই যেতে চাইছে না। আমার কাছে খবর আছে সরকার খুব কড়া হাতে ওদের মোকাবিলা করার জন্য তৈরি হচ্ছে এখন।”
“ওঃ, সেই উদ্বাস্তু সমস্যা!” বললেন ডাক্তার। “যতসব ঝামেলা। তো, আপনার স্বামীর তাতে কী? ওই দ্বীপে ওনার চেনাশুননা কেউ আছে নাকি? ওনার সঙ্গে ওদের সম্পর্কটা কী?”
এক মুহূর্ত চুপ করে রইল নীলিমা। তারপর গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে একটু দ্বিধার সঙ্গে বলল, “আপনাকে ব্যাপারটা আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না ডাক্তারবাবু। আমার স্বামী যখন রিটায়ার করলেন, তারপর থেকেই ওঁর হাতে আর বিশেষ কোনও কাজ তো নেই–তাই উনি ওই মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের ভালমন্দের সঙ্গে আস্তে আস্তে জড়িয়ে ফেলেছেন নিজেকে। এখন আমাদের যে সরকার আছে তারা ওদের বিরুদ্ধে কিছু করবে সেটা উনি ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারেন না। উনি সেই আগেকার আমলের বামপন্থী মানুষ। আজকালকার অনেকের মতো নন, এখনও উনি মনেপ্রাণে ওই আদর্শে বিশ্বাস করেন। এদিকে, এখন যারা ক্ষমতায় আছে তারা অনেকেই ওঁর এক সময়কার বন্ধু বা রাজনৈতিক সহকর্মী। আসলে–কী বলব–আমার স্বামী ঠিক প্র্যাকটিকাল মানুষ নন, বাস্তব জগৎটার সম্পর্কে ওঁর ধারণা খুব সীমিত। উনি বুঝতে পারেন না, একটা পার্টি যখন ক্ষমতায় আসে তাকে রাজ্যশাসনের কাজ করতে হয়। তার কতগুলি সীমাবদ্ধতা থাকে। আমি ভয় পাচ্ছি মরিচঝাঁপিতে যা ঘটতে যাচ্ছে সেটা যদি উনি জানতে পারেন, সে মোহভঙ্গের আঘাত উনি সহ্য করতে পারবেন না–ওঁর পক্ষে মারাত্মক হয়ে দাঁড়াতে পারে সেটা।”
“তা হলে সেসব ওনাকে না জানানোই ভাল,” ডাক্তারের গলা শোনা গেল। “কী করতে কী করে বসবেন, বলা তো যায় না।”
“একটা কথা বলুন ডাক্তারবাবু,” নীলিমা বলল, “কয়েকদিন কি ওঁকে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা যায় না?”
“তা যায়। সেটাই মনে হয় ভাল হবে।”
আর কিছু শোনার ছিল না আমার। পড়ার ঘরে ফিরে গিয়ে চটপট কয়েকটা জিনিস ঝোলায় পুরে নিলাম। তারপর চুপি চুপি নেমে এসে তাড়াতাড়ি হাঁটা দিলাম গ্রামের দিকে। ভাগ্যক্রমে ঘাটে একটা নৌকো ছিল তখন, তাতে করে সোজা চলে গেলাম সাতজেলিয়া–হরেনের খোঁজে।
“এক্ষুনি আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে হরেন,” দেখা হতেই ওকে বললাম। “সরকার মরিচঝাঁপি আক্রমণ করবে ঠিক করেছে, খবর পেয়েছি আমি।”
খবর ওর কাছেও কিছু কম ছিল না। নানারকম গুজব ওরও কানে এসেছে–বাসভর্তি লোক বাইরে থেকে এসে নাকি জড়ো হয়েছে মরিচঝাঁপির আশেপাশের গ্রামগুলিতে, গুণ্ডা-মস্তান ধরনের লোক সব। ভাটির দেশের মানুষ এরকম লোক আগে কখনও দেখেনি। পুলিশের নৌকো সবসময় টহল দিচ্ছে দ্বীপের চারদিকে; ঢোকা কি বেরোনো প্রায় অসম্ভব।
“হরেন, কুসুম আর ফকিরকে ওখান থেকে বের করে আনতেই হবে আমাদের। এই অঞ্চলের নদীনালা তোমার থেকে ভাল কেউ চেনে না। ওখানে গিয়ে পৌঁছনোর কোনও একটা পথ বের করা যাবে না?” ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি।
মিনিটখানেক কী চিন্তা করল হরেন। তারপর বলল, “আজ চাঁদ থাকবে না আকাশে। যাওয়া গেলেও যেতে পারে। চেষ্টা করে দেখি একবার।”
সন্ধের মুখে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। বেশ খানিকটা খাবার আর জল নিয়ে নিলাম সঙ্গে। খানিক পরেই অন্ধকার ঘনিয়ে এল। আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু হরেন তারই মধ্যে কী করে যেন ঠিক চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নৌকোটাকে। খুব ধীরে ধীরে চলছিলাম আমরা, একেবারে পাড় ঘেঁষে। কথাবার্তা বলছিলাম ফিসফিস করে।
“আমরা এখন কোথায় হরেন?” জিজ্ঞেস করলাম আমি।
ও দেখলাম একেবারে নিখুঁতভাবে বলে দিল আমাদের অবস্থান। “এই গারল পেরিয়েছি। ঝিল্লায় ঢুকেছি এবার। বেশি দূর নেই আর, একটু পরেই পুলিশের নৌকো দেখতে পাবেন।” মিনিট কয়েক পরেই দেখতে পেলাম বোটগুলোকে–সগর্জনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সার্চলাইটের আলোয় ধুয়ে দিচ্ছে নদীটাকে। প্রথমে একটা, তারপর আরেকখানা, তারপর আরও একটা। খানিকক্ষণ পাড় ঘেঁষে চুপটি করে লুকিয়ে রইলাম আমরা। কতক্ষণ পরপর বোটগুলো আসছে সে সময়টা মনে মনে মেপে নিল হরেন। তারপর আবার রওয়ানা হলাম। খানিক চলে, খানিক থেমে একটা সময় পুলিশ-নৌকোর নজরদারির এলাকা পেরিয়ে গেলাম আমরা।
একটু বাদেই গোত্তা খেয়ে পাড়ের নরম মাটিতে গিয়ে ঠেকল আমাদের নৌকো। “এসে গেছি সার,” জানান দিল হরেন। “পৌঁছে গেছি মরিচঝাঁপিতে।”দু’জনে মিলে টেনেটুনে ডিঙিটাকে বাদাবনের আড়ালে নিয়ে গিয়ে তুললাম–যাতে জল থেকে চোখে না পড়ে। হরেন বলল দ্বীপের লোকেদের সব নৌকো পুলিশ নাকি ডুবিয়ে দিয়েছে। আমাদের নৌকোটা তাই ভাল করে ঢেকেঢুকে আড়াল করে রাখলাম, তারপর জল আর খাবার-দাবার যা যা সঙ্গে এনেছিলাম সেগুলি নিয়ে নদীর পাড় দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছলাম কুসুমের কুঁড়েতে। সেখানে পৌঁছে আমরা তো অবাক। কুসুমের কোনও হেলদোলই নেই। দিব্বি আছে এখনও। সারা রাত ধরে আমরা ওকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম–এক্ষুনি ওর চলে যাওয়া উচিত দ্বীপ ছেড়ে, কিন্তু কোনও কথাই ও কানে তুলল না।
“মরিচঝাঁপি ছেড়ে কোথায় যাব? আর কোথাও তো আমি যেতে চাই না,” ওর সাফ জবাব। কী কী গুজব আমাদের কানে এসেছে ওকে বললাম, বললাম চারপাশের সব কটা গাঁয়ে বাইরে থেকে তোক এসে জড়ো হয়েছে, যে-কোনও সময়ে হামলা শুরু হয়ে যাবে। হরেন নিজের চোখে দেখেছে, বাস ভর্তি করে এসেছে সব। “কী করবে ওরা?” কুসুম বলল। “এখনও দশ হাজারের বেশি লোক আমরা এখানে আছি। ভরসা করে থাকতে হবে। হাল ছাড়লে চলবে কেন?”
“কিন্তু ফকিরের কী হবে?” জিজ্ঞেস করলাম আমি। “ভালমন্দ একটা কিছু যদি ঘটে যায়, ও তা হলে কী করবে?”
“ঠিক বলেছেন সার,” আমার সঙ্গে সুর মেলাল হরেনও। “তুই যদি না যেতে চাস, তা হলে ফকিরকে অন্তত দিয়ে দে আমার সঙ্গে। কয়েকটা দিন অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে রাখি, তারপর এখানকার ঝামেলা-টামেলা মিটে গেলে আবার এসে দিয়ে যাব।”
বোঝা গেল এই নিয়ে আগে থাকতেই ভেবে রেখেছিল কুসুম। বলল, “ঠিক আছে তা হলে, তাই করা যাক। ফকিরকে নিয়ে যাও তোমরা, সাতজেলেতে নিয়ে কয়েকদিন রাখো, তারপর এখানকার ঝড়ঝাঁপটা থামলে নিয়ে এসো আবার।”
কথা বলতে বলতে ফর্সা হয়ে গিয়েছিল আকাশ। আর ফেরা যাবে না এখন। হরেন বলল, “রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। অন্ধকার না হলে পুলিশ বোটের নজর এড়িয়ে বেরোতে পারব না।”
এবার আমার পালা ওদের অবাক করে দেওয়ার। বললাম, “হরেন, আমি কিন্তু থেকেই যাচ্ছি।”
ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেল ওরা। বিশ্বাসই করতে পারছিল না। বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগল কেন আমি থেকে যেতে চাই, কিন্তু আমি সেসব কথা এড়িয়ে গেলাম। কত কিছুই তো ওদের বলতে পারতাম আমি লুসিবাড়িতে আমার জন্য যে ওষুধের ব্যবস্থা করা আছে সে কথা বলতে পারতাম, নীলিমার সঙ্গে ডাক্তারের কথোপকথনের কথা বলতে পারতাম অথবা দিনের পর দিন কী শূন্যতাবোধ নিয়ে সময় কাটিয়েছি আমার পড়ার ঘরটায় সেই কথাও বলতে পারতাম। কিন্তু এসব কিছুর বিন্দুমাত্র গুরুত্ব আছে বলে মনে হল না আমার। ঘটনা হল মরিচঝাঁপিতে আমার থেকে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে এতটুকু কোনও সংশয় ছিল না আমার মনে। এই নোটবইটা দেখিয়ে বললাম, “আমাকে থাকতেই হবে রে, একটা জরুরি লেখা লিখে ফেলতে হবে এখানে বসে।”
আর সময় নেই। মোমবাতিটা দপদপ করছে। পেনসিলটা ছোট্ট হয়ে গেছে ক্ষয়ে ক্ষয়ে। আমি শুনতে পাচ্ছি ওরা এগিয়ে আসছে। আশ্চর্য মনে হচ্ছে হো হো করে হাসতে হাসতে আসছে ওরা। হরেন এক্ষুনি বেরিয়ে যেতে চাইবে জানি, কারণ রাত আর বেশি বাকি নেই। ভাবতেই পারিনি এই গোটা নোটবইটা লিখে শেষ করে ফেলতে পারব আমি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখছি পুরোটা ভরেই গেল। এটাকে এখানে রেখে আর লাভ নেই। ঠিক করেছি দিয়ে দেব হরেনের সঙ্গে, যাতে কোনও না কোনও সময় তোমার হাতে গিয়ে পৌঁছয় এটা, কানাই। আমি নিশ্চিত জানি সারাজীবনে জগতের যেটুকু মনোযোগ আমি আকর্ষণ করতে পেরেছি, তার থেকে অনেক বেশি তুমি পারবে। এই খাতা নিয়ে কী করবে সেটা তুমিই ঠিক কোরো। আমি সবসময় তরুণদের ওপর ভরসা রেখে এসেছি। আমার প্রজন্মের মানুষদের তুলনায় তোমরা আদর্শের দিক দিয়ে ঋদ্ধতর হবে, কম শুভনাস্তিক হবে, কম স্বার্থপর হবে–এ আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি।
ওরা ভেতরে ঢুকে এসেছে। মোমের আলোয় ওদের মুখগুলো দেখতে পাচ্ছি আমি। ওদের হাসিতে আমি কবির সেই পংক্তিগুলি প্রত্যক্ষ করছিঃ
‘দেখো, আমি বেঁচে আছি। কোন পথ্যে? শৈশব অথবা ভাবীকাল,
কোনওটাই হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না… অস্তিত্বের অনন্ত পর্যায়
আমার হৃদয় থেকে উৎসারিত।’
খাতাটা রাখতে গিয়ে কানাই দেখল হাত কাঁপছে ওর। লফের ধোঁয়ায় ভরে গেছে কেবিন, কেরোসিনের গন্ধ চারিদিকে; মনে হল দম বন্ধ হয়ে আসছে। শোয়ার জায়গা থেকে একটা কম্বল তুলে গায়ে পেঁচিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এল কেবিন থেকে। বাইরে বেরোতেই ধক করে কড়া বিড়ির গন্ধ এসে লাগল নাকে। বাঁদিকে ফিরে বোটের সামনের দিকটায় তাকাল কানাই।
সেখানে পাশাপাশি পাতা দুটো আরাম চেয়ার। তার একটায় বসে আছে হরেন। পা দুটো বোটের গলুইয়ের কাছে রেখে বিড়ি টানছে। কানাই কেবিনের দরজা বন্ধ করতে ফিরে তাকাল ও।
“এখনও জেগে?”
“হ্যাঁ, কানাই বলল। “এইমাত্র মেসোর খাতাটা পড়ে শেষ করলাম।”
জবাবে আবেগহীন একটা আওয়াজ করল হরেন গলা দিয়ে।
হরেনের পাশের চেয়ারটায় গিয়ে বসল কানাই। “আপনার নৌকোয় ফকিরকে নিয়ে ফিরে আসার কথা দিয়েই শেষ হয়েছে মেসোর লেখা।”
চোখটা একটু নামাল হরেন, জলের দিকে। যেন ফিরে তাকাল অতীতের ভেতর। খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, “আরেকটু আগেই বেরিয়ে পড়া উচিত ছিল আমাদের। জলের টানের সুযোগটা পাওয়া যেত তা হলে।”
“আর মরিচঝাঁপিতে তারপর কী হল? আপনি জানেন?” বিড়িতে আরেকটা টান দিল হরেন। “আর সবাই যা জানে তার থেকে বেশি কিছু আমি জানি না। সবই গুজব বলতে পারেন।”
“কী গুজব?”
অল্প একটু ধোঁয়া পাক খেয়ে বেরিয়ে এল হরেনের নাক দিয়ে। “শুনেছিলাম হামলাটা শুরু হয়েছিল তার পরের দিন। আশেপাশের গাঁ-গুলোতে যেসব গুণ্ডারা জড়ো হয়েছিল তাদের সকলকে লঞ্চে, ডিঙিতে, ভটভটিতে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল মরিচঝাঁপিতে। ওরা গিয়ে সব ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিল, দ্বীপের লোকেদের নৌকো-টৌকো যা ছিল ডুবিয়ে দিল, খেতখামার সব নষ্ট করে দিল।” স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে গলা দিয়ে একটা আওয়াজ করল হরেন। “যা যা করা যায় তার কোনওটাই বাকি রাখেনি।”
“তা হলে কুসুম আর আমার মেসো–ওদের কী হল?”
“ঠিক কী যে হল সেটা কেউই জানে না। তবে আমি যতটা শুনেছিলাম তা হল, একদল মেয়েকে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়েছিল ওরা। কুসুম তাদের মধ্যে ছিল। লোকে বলে ওদের ওপরে অত্যাচার করে তারপর নাকি নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, যাতে ভেসে যায় স্রোতের টানে। বেশ কিছু মানুষ মারা গিয়েছিল মরিচঝাঁপিতে সেদিন। সাগর টেনে নিয়েছিল ওদের সবাইকে।”
“আর আমার মেসোর কী হল?”
“অন্য অনেকের সঙ্গে ওনাকেও একটা বাসে তুলে দেওয়া হয়েছিল। ওই মধ্যপ্রদেশ না কোথায়, যেখান থেকে ওরা এসেছিল সেখানে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু কোথাও একটা এসে নিশ্চয়ই ছেড়ে দিয়েছিল ওনাকে, কারণ শেষপর্যন্ত তো উনি ক্যানিং-এ গিয়ে পৌঁছেছিলেন।”
এই পর্যন্ত বলে হরেন নিজের পকেট হাতড়াতে শুরু করল। বেশ খানিকক্ষণ চলল পকেটের ভেতর ওর খোঁজাখুঁজি। বিড়বিড় করে গালি দিতে লাগল নিজের মনে। অবশেষে পকেট থেকে যখন বিড়িটা বের করল, ততক্ষণে কানাইয়ের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে নির্মল আর কুসুমের প্রসঙ্গ থেকে কথা ঘোরানোর চেষ্টা করছে হরেন। খানিক পরে তাই বেশ একটা অমায়িক গলায় যখন জিজ্ঞেস করল, “কালকে তা হলে কখন রওয়ানা হবেন ভাবছেন?” কানাই আশ্চর্য হল না।
কিন্তু হরেনকে কথা ঘোরাতে দেবে না ও ঠিক করেছে। “আচ্ছা, একটা কথা বলুন হরেনদা, আপনিই তো আমার মেসোকে মরিচঝাঁপি নিয়ে গিয়েছিলেন; মেসো ওই জায়গাটার সঙ্গে এতটা জড়িয়ে পড়েছিলেন কেন বলুন তো? আপনার কী মনে হয়?”
“জড়িয়ে তো কমবেশি সবাই পড়েছিল তখন,” ঠোঁট ওলটাল হরেন।
“কিন্তু ধরুন, কুসুম আর ফকির আপনার আত্মীয় ছিল। ওদের জন্য আপনার ভাবনা হতে পারে–সেটা আমি বুঝতে পারি। কিন্তু সারের ব্যাপারটা কী? ওনার কাছে কেন এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল মরিচঝাঁপির ঘটনাটা?”
চুপ করে বিড়ি টানতে লাগল হরেন। অবশেষে বলল, “আপনার মেসো অন্য আর পাঁচটা মানুষের মতো ছিলেন না কানাইবাবু। লোকে বলত ওনার মাথায় গণ্ডগোল ছিল। আর পাগলে কী না করে ছাগলে কী না খায়, কে বলতে পারে বলুন?”
“একটা কথা বলুন হরেনদা,” কানাই নাছোড়বান্দা, “এরকম কি হতে পারে যে মেসো কুসুমের প্রেমে পড়েছিলেন?”
উঠে পড়ল হরেন। নাকঝাড়া দিয়ে এমন একটা ভাব করল যে পরিষ্কার বোঝা গেল সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে ওর। বিরক্ত কাটাকাটা গলায় তারপর বলল, “দেখুন কানাইবাবু, আমি মুখুসুখু মানুষ। আপনি যা বলছেন সেসব কথা আপনারা শহুরে লোকেরা ভাবতে পারেন, কিন্তু আমার ওসব ভাবার মতো সময় নেই।”
টান মেরে বিড়িটা দূরে ছুঁড়ে ফেলল হরেন। ঘঁাৎ করে আগুন নেভার শব্দ কানে এল। “যান, গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন এখন,” বলল হরেন। “কাল সকাল সকাল বেরোতে হবে।”