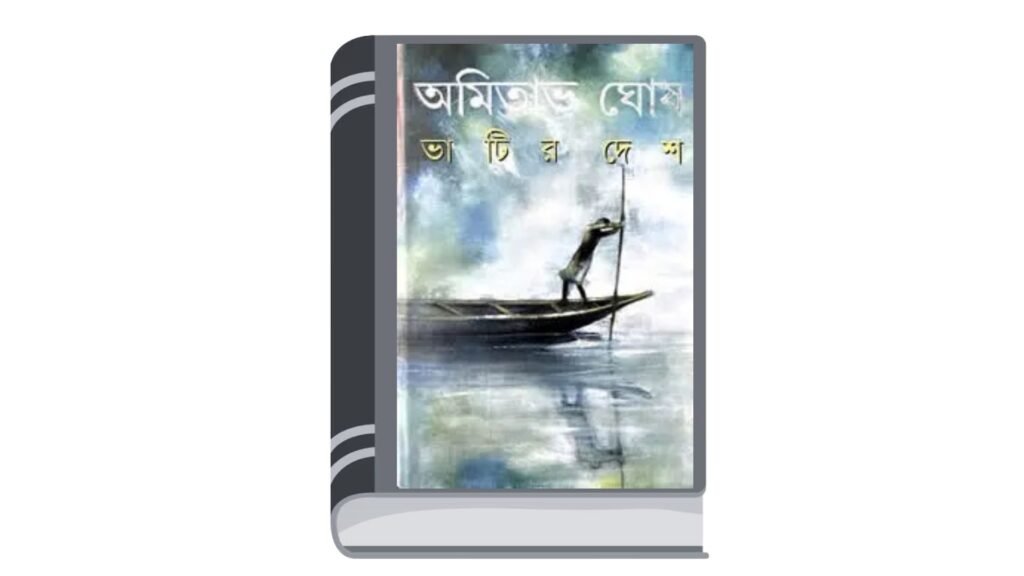২.৩ দ্বিতীয় পর্ব – জোয়ার
রবিবারের ডাকঘর
সকাল সকালই শুয়ে পড়েছিল পিয়া। মাঝরাত্রে ঘুমটা চটে গেল হঠাৎ, উঠে বসে পড়ল বাঙ্কের ওপর। কয়েকটা মিনিট ধরে চেষ্টা করল যদি আবার ঘুম আসে। লাভ হল না। হাল ছেড়ে দিয়ে কম্বলটা গায়ে পেঁচিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এল ডেকের উপর। চাঁদের আলোয় ধুয়ে যাচ্ছে চারদিক। এত ফটফটে জ্যোৎস্না, যে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে গেল ও, পিটপিট করে সইয়ে নিতে হল চোখ। একটু অবাক হয়ে দেখল কানাইও বসে আছে বাইরে। ছোট একটা কেরোসিন লণ্ঠনের আলোয় কী পড়ছে একমনে। এগিয়ে গিয়ে অন্য চেয়ারটায় বসে পড়ল পিয়া। বলল, “এখনও জেগে? মেশোর নোটবুকটা পড়ছেন বুঝি?”
“হ্যাঁ। পড়া আসলে হয়ে গেছে, আরেকবার উলটে পালটে দেখছিলাম।”
“আমি একটু দেখতে পারি?”
“নিশ্চয়ই।” খাতাটা বন্ধ করে পিয়ার দিকে এগিয়ে দিল কানাই। আলগোছে নোটবইটা নিয়ে খুলে ধরল পিয়া।
“খুব খুদে খুদে লেখা।”
“হ্যাঁ,” বলল কানাই। “পড়া একটু কঠিন।”
“বাংলায় লেখা, তাই না?”
“হ্যাঁ।” সাবধানে খাতাটা বন্ধ করে কানাইকে ফিরিয়ে দিল পিয়া। “কী আছে এর মধ্যে?” মাথা চুলকোল কানাই। নোটবইয়ের বিষয়বস্তু কীভাবে বর্ণনা করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। “কী নিয়ে মানে… নানারকম বিষয় নিয়েই লেখা আছে; বিভিন্ন জায়গার কথা, অনেক সব লোকেদের কথা, এইসব আর কী–”।
“সেসব লোকেদের কাউকে আপনি চেনেন?”
“চিনি। আমাদের ফকিরের মাকে নিয়েও অনেক কথা লেখা আছে এই নোটবইতে। ফকিরের কথাও আছে–তবে মেসো ওকে যখন দেখেছিলেন তখন ও খুবই ছোট।”
বিস্ময়ে চোখ গোল গোল হয়ে গেল পিয়ার। “ফকির আর ওর মা? ওদের কথা কী করে এল?”
“আপনাকে বলেছিলাম না, যে কুসুম–ফকিরের মা–এখানকার একটা দ্বীপে বসতি তৈরির একটা চেষ্টার সঙ্গে জড়িত ছিল?”
“তা বলেছিলেন।”
হাসল কানাই। “মনে হয় নিজের অজান্তেই খানিকটা কুসুমের প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন আমার মেসো।”
“তাই লিখেছেন উনি এই খাতায়?”
“না,” জবাব দিল কানাই। “কিন্তু সে উনি লিখতেনও না।”
“কেন?”
“উনি যেরকম ছিলেন, যে যুগের যে জায়গার মানুষ ছিলেন–তাতে এরকম কিছু লেখাটাকে বাঁচালতা মনে করতেন হয়তো,” কানাই বলল।
নিজের ছোট ছোট কেঁকড়া চুলে আঙুল বোলাল পিয়া। “বুঝলাম না ঠিক। আচ্ছা, উনি কী ধরনের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন?”
চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল কানাই। প্রশ্নটা ভাবতে সময় নিল একটু। তারপর বলল, “একটা সময় উনি ছিলেন প্রগতিবাদী। এমনকী এখনও যদি আপনি আমার মাসিকে জিজ্ঞেস করেন, মাসি বলবেন মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের সঙ্গে মেসো জড়িয়ে পড়েছিলেন কারণ বিপ্লবের ভূতটাকে উনি মাথা থেকে কখনও তাড়াতে পারেননি।”
“আপনি মনে হচ্ছে মাসির সঙ্গে একমত নন?”
“না,” জবাব দিল কানাই। “আমার মনে হয় মাসির ধারণাটা ভুল। আমার চোখে মেসোর ঘাড়ে যে ভূত ভর করেছিল তা রাজনীতির নয়, শব্দবাক্য-অক্ষরের। কিছু কিছু মানুষ থাকে দেখবেন যারা কবিতার জগতেই জীবন কাটায়। আমার মেসো ছিলেন সেইরকম একজন লোক। মাসির পক্ষে এরকম মানুষকে বুঝে ওঠাটা কঠিন ছিল কিন্তু মেসোর ধরনটাই ছিল ওই। কবিতা পড়তে ভালবাসতেন উনি, বিখ্যাত জার্মান কবি রাইনের মারিয়া রিলকের কবিতা। আমাদের কয়েকজন নামকরা কবি সেসব কবিতা বাংলায় অনুবাদ করেছেন। রিলকে বলেছিলেন, ‘জীবন যাপিত হয় পরিবর্তনে’, আর আমার মনে হয় কবির এই কথাটা মেসো মর্মে মর্মে গেঁথে নিয়েছিলেন–কাপড় যেমন কালি শুষে নেয়, সেইভাবে। ওঁর কাছে কুসুম ছিল রিলকের সেই পরিবর্তনের ধারণার মূর্ত রূপ।”
“মার্ক্সবাদ আর কবিতা?” ভুরু তুলে শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করল পিয়া। “একটু অদ্ভুত কম্বিনেশন–না?”
“তা ঠিক,” কানাই সায় দিল। “আসলে এই ধরনের পরস্পর বিরোধিতাগুলি ছিল ওঁদের প্রজন্মের বৈশিষ্ট্য। যেমন, মেসোর মতো বস্তুবোধশূন্য মানুষ আমি দুটো দেখিনি, কিন্তু নিজেকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদী বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে ভালবাসতেন উনি।”
“তার মানেটা ঠিক কী?”
“ওঁর কাছে তার মানে হল, এ জগতে সমস্ত কিছুই পরস্পর সম্পর্কিত–গাছপালা, আকাশ, জল-হাওয়া, মানুষ-জন, কাব্য-কবিতা, বিজ্ঞান, প্রকৃতি–সবকিছু। খুঁজে খুঁজে তথ্য সংগ্রহ করতেন মেসো সবসময়, অনেক পাখি যেমন চকচকে কিছু দেখলেই চুরি করে নিয়ে গিয়ে বাসায় জড়ো করে, তেমনি। কিন্তু সেসব তথ্য যখন উনি একসঙ্গে গেঁথে তুলতেন, সেগুলো হয়ে উঠত একেকটা গল্প–এক ধরনের কাহিনি।”
হাতের মুঠোয় চিবুকের ভর রেখে বসল পিয়া। “যেমন?”
মিনিট খানেক ভাবল কানাই। “মেসোর বলা একটা গল্প আমার এক্ষুনি মনে পড়ছে–কিছুতেই ভুলতে পারি না আমি গল্পটা।”
“কী নিয়ে সেটা?”
“ক্যানিং-এর কথা মনে আছে আপনার, গঞ্জ মতো যে জায়গাটায় এসে ট্রেন থেকে নামলাম আমরা?”
“কেন মনে থাকবে না?” পিয়া বলল। “ওখানেই তো পারমিটটা পেলাম আমি। আমার অবশ্য জায়গাটাকে খুব একটা স্মরণীয় স্থান বলে মনে হয়নি।”
“ঠিকই বলেছেন,” বলতে লাগল কানাই। “আমি প্রথম ওখানে যাই ১৯৭০ সালে, মেসো আর মাসির সঙ্গে লুসিবাড়ি আসার পথে। জঘন্য লেগেছিল জায়গাটা আমার মনে হয়েছিল বীভৎস কাদা-প্যাঁচপ্যাটে ছোট শহর একটা। সেইরকমই একটা কিছু বোধহয় বলেছিলাম আমি। আর মেসো তো সঙ্গে সঙ্গে খেপে আগুন। প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন আমার ওপর, একটা জায়গা কীরকম সেটা নির্ভর করে তুমি তাকে কীভাবে দেখছ তার ওপর। তারপর একটা গল্প বললেন আমাকে। এমন অদ্ভুত গল্প, যে আমি ভাবলাম সেটা বুঝি তক্ষুনি বানালেন মুখে মুখে। কিন্তু পরে যখন বাড়ি ফিরে গেলাম, সত্যি সত্যিই বইপত্র ঘেঁটে দেখেছিলাম আমি–এক বিন্দুও বানিয়ে বলেননি মেসো।”
“কী ছিল গল্পটা?” জিজ্ঞেস করল পিয়া। “মনে আছে আপনার? আমার শুনতে ইচ্ছে করছে।”
“বেশ। মেসো যেমন যেমন বলেছিলেন সেভাবেই আমি আপনাকে বলার চেষ্টা করছি,” কানাই বলল। “কিন্তু একটা ব্যাপার আপনাকে মনে রাখতে হবে–মেসো গল্পটা বলেছিলেন বাংলায়। আমি কিন্তু মনে মনে অনুবাদ করে সেটা বলব আপনাকে।”
“হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন আপনি।”
আকাশের দিকে তর্জনী তুলে বলতে শুরু করল কানাই: “ঠিক আছে তা হলে বন্ধুগণ, আমি বলছি, তোমরা মন দিয়ে শোনো। আমি এখন তোমাদের বলব মাতলা নদীর কথা, এক ঝড়ে-পাওয়া মাতালের কথা, আর ক্যানিং নামে এক লাটসাহেবের মাতলামির কথা। শোনো, কান পেতে শোনো।
.
এই ভাটির দেশের অন্য আরও অনেক জায়গার মতোই ক্যানিং-এর নামও দিয়েছিলেন একজন ইংরেজ সাহেব। সে সাহেব আবার যে সে সাহেব নয়, একেবারে লাটসাহেব–ভাইসরয় লর্ড ক্যানিং। এই লাটসাহেব আর তার লেডি দেশজুড়ে যেখানে সেখানে নিজেদের নাম ছড়িয়ে বেড়াতে ভালবাসতেন। তাদের পরবর্তী প্রজন্মের রাজনীতিকরা যেমন নিজেদের ছাই ছড়াতে পছন্দ করতেন, অনেকটা সেইরকম। অদ্ভুত অদ্ভুত সব জায়গার নাম আছে এই সাহেব-মেমের নামে রাস্তার নাম, জেলের নাম, পাগলাগারদের নাম। মজার ব্যাপারও অনেক হত। যেমন, লেডি ক্যানিং ছিলেন লম্বা, রোগা, একটু বদমেজাজি, কিন্তু কলকাতার এক মিঠাইওয়ালার মাথায় কী খেলল কে জানে, নতুন একটা মিষ্টি তৈরি করে তার নাম দিয়ে দিল মেমসাহেবের নামে। সে মিঠাই কিন্তু গোল, কালো আর রসে টইটম্বুর–মানে লেডি ক্যানিং-এর চেহারা কি স্বভাব কোনওটার সঙ্গেই কোনও মিল নেই তার। তবুও কপাল খুলে গেল মিষ্টিওয়ালার। হু হু করে বিক্রি হতে লাগল তার আবিষ্কৃত সেই নতুন মিঠাই। এত পরিমাণে লোকে সে মিষ্টি খেতে লাগল যে ‘লেডি ক্যানিং’–এই পুরো কথাটা উচ্চারণ করতে যে সময় লাগে সে সময়টাও দিতে চাইল না তারা। মুখে মুখে মিষ্টিটার নাম হয়ে দাঁড়াল ‘লেডিগেনি’।
এখন, লোকের মুখে ভাষা এবং শব্দের পরিবর্তনের নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম আছে। সেই নিয়মে যদি লেডি ক্যানিং হয়ে দাঁড়ায় লেডিগেনি, পোর্ট ক্যানিং-এর নামও তা হলে আস্তে আস্তে পালটে পোটুগেনি বা পোডগেনি হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, তাই না? কিন্তু দেখ বন্ধুগণ, এই বন্দর শহরের নাম কিন্তু অপরিবর্তিত রয়ে গেল। এখনও মানুষ ওই লাটসাহেবের নামেই চেনে ক্যানিংকে।
কিন্তু কেন? কেন একজন লাটসাহেব তার সুখের সিংহাসন ছেড়ে এই মাতলার কাদায় এসে নিজের নামের চাষ করতে গেলেন?
মহম্মদ বিন তুঘলকের কথা মনে আছে তো তোমাদের? সেই পাগলা বাদশা, যিনি দিল্লি শহর ছেড়ে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এক অজ পাড়াগাঁয়? সেই একই ভূতে ধরেছিল বিলিতি সাহেবদেরও। একদিন হঠাৎ ওরা ঠিক করল নতুন একটা বন্দর চালু করতে হবে, বাংলাদেশের একটা নতুন রাজধানীর প্রয়োজন–দ্রুত পলি জমছে কলকাতার হুগলি নদীতে, ওদের তাই মনে হল কলকাতা বন্দরের ডকগুলি আর কিছুদিনের মধ্যেই বুজে যাবে কাদায়। যথারীতি, সব প্ল্যানার আর সার্ভেয়াররা বেরিয়ে পড়ল দলে দলে, পরচুলা আর চাপা পাতলুন পরে চষে বেড়াতে লাগল সারা রাজ্য, মাপজোক আর ম্যাপ তৈরি শুরু হয়ে গেল পুরো দমে। অবশেষে, এই মাতলার তীরে এসে একটা জায়গা পছন্দ হল ওদের। জেলেদের ছোট্ট একটা গ্রাম, তার সামনে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে নদী, আর সে নদী এমন চওড়া যে দেখলে মনে হয় সোজা সাগর পর্যন্ত বিছানো এক রাজপথ।
এখন, এটা তো সবাই জানে যে বাংলায় মাতলা’ কথাটার মানে মত্ত। আর এ নদীকে যারা চেনে তারা ভালই জানে কেন এর এই নাম। কিন্তু নাম আর শব্দ নিয়ে মাথা ঘামানোর এত সময় কোথায় সেই ইংরেজ টাউন প্ল্যানারদের? সোজা লাটসাহেবের কাছে ফিরে গিয়ে তাঁকে জানাল কী চমৎকার জায়গা একখানা খুঁজে পাওয়া গেছে। শোনাল কেমন বিশাল চওড়া আর গভীর নদী, সোজা গিয়ে মিশেছে সাগরে, তার পাশে কেমন সুন্দর টানা সমতল জায়গা; লাটসাহেবকে তাদের প্ল্যান আর ম্যাপ-ট্যাপ যা যা ছিল দেখাল, সেখানে কী কী বানানোর পরিকল্পনা আছে শোনাল তাঁকে–হোটেল, বেড়ানোর জায়গা, পার্ক, বিরাট বিরাট প্রাসাদ, ব্যাঙ্ক, রাস্তাঘাট আরও কত কী। ওঃ, দারুণ সুন্দর একখানা শহর গড়া যাবে ওই মাতলার তীরে–কোনও কিছুর কোনও অভাব থাকবে না বাংলার সেই নতুন রাজধানীতে।
ঠিকাদারদের ডেকে সব বুঝিয়ে-টুঝিয়ে দেওয়া হল, কাজও শুরু হয়ে গেল চটপট: হাজার হাজার মিস্ত্রি, মহাজন আর ওভারসিয়াররা এসে জড়ো হল মাতলার পাড়ে, শুরু করল খোঁড়াখুঁড়ি। মাতলার জল খেয়ে মাতালের মতো কাজ করতে লাগল তারা, সব বাধা তুচ্ছ করে–এমনকী ১৮৫৭-র বিদ্রোহের সময়ও বন্ধ হল না কাজ। তোমরা যদি তখন এই মাতলার পাড়ে থাকতে বন্ধুগণ, তোমরা জানতেও পারতে না যে উত্তর ভারতে কেমন গ্রাম থেকে গ্রামে খবর চালাচালি হচ্ছে চাপাটির সঙ্গে, মঙ্গল পাণ্ডে কখন বন্দুক ঘুরিয়ে ধরেছে তার অফিসারদের দিকে, কাতারে কাতারে কোথায় খুন হয়ে যাচ্ছে নারী শিশু, কোথায় বিদ্রোহীদের উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে কামানের মুখে বেঁধে। এখানে প্রশান্ত নদীর পারে কাজ চলতে লাগল অবিশ্রাম: বাঁধ তৈরি হল, ভিত খোঁড়া হল, নদীর ধার ঘেঁষে বানানো হল রাস্তা, বসানো হল রেলের লাইন। এবং এই পুরো সময়টা ধরে শান্ত ধীর গতিতে বয়ে চলল মাতলা, অপেক্ষা করে রইল। কিন্তু নদীও সব সময় তার সব গোপন কথা আড়াল করে রাখতে পারে না। এখানে যখন বন্দর তৈরির কাজ চলছিল, ঠিক সেই সময় কলকাতা শহরে বাস করতেন এক ভদ্রলোক, স্বভাব তারও অনেকটা এই মাতলা নদীরই মতো। সামান্য একটা শিপিং ইন্সপেক্টরের চাকরি করতেন তিনি ইংরেজ সাহেব, নাম হেনরি পিডিংটন। ভারতে আসার আগে এই পিডিংটন সাহেব কয়েক বছর কাটিয়েছিলেন ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে। সেখানকারই কোনও এক দ্বীপে থাকার সময় প্রেমে পড়েছিলেন সাহেব। না, কোনও মহিলাকে ভালবাসেননি ভদ্রলোক, এমনকী এরকম নির্জন জায়গায় বেশিদিন কাটালে অনেক সাহেব যেমন পাগলের মতো তাদের কুকুরকে ভালবাসে, সেরকমও কিছু ঘটেনি তার জীবনে। মিস্টার পিডিংটন সেখানে ঝড়ের প্রেমে পড়েছিলেন। ওই সব দ্বীপে সে ঝড়ের নাম ছিল হারিকেন, আর সেই হারিকেনকেই ভীষণ ভালবেসে ফেললেন সাহেব। অনেক লোক যেমন পাহাড় বা আকাশের তারা ভালবাসে, পিডিংটনের ভালবাসা কিন্তু ঠিক সেরকম ছিল না। ঝড় ছিল তার কাছে বইয়ের মতো, সংগীতের মতো। প্রিয় লোক বা : গায়কের প্রতি যেরকম একটা টান থাকে মানুষের, ক্যারিবিয়ানের তুফান ঠিক সেইভাবে টানত সাহেবকে। পিডিংটন ঝড়কে পড়তেন, শুনতেন, বুঝতে চেষ্টা করতেন, ঝড় নিয়ে চর্চা করতেন। ঝড়কে এত ভালবাসতেন উনি যে নতুন একটা নামই তৈরি করে ফেললেন–‘সাইক্লোন’।
এখন, আমাদের কলকাতা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মতো অতটা রোমান্টিক জায়গা হতে পারে, কিন্তু পিডিংটন সাহেবের প্রণয়চর্চার জন্য এ শহরও কোনও অংশে খারাপ ছিল না। ঝড়ের ভয়াল রূপের হিসাবে যদি বিচার করা যায়, দেখা যাবে বঙ্গোপসাগরের স্থান অন্য সব সমুদ্রের ওপরে–সে ক্যারিবিয়ান সাগরই হোক, কি দক্ষিণ চিন সমুদ্র। আমাদের এই সাগরের তুফান থেকেই তো ‘টাইফুন’ শব্দটা তৈরি হয়েছে, তাই না?
লাটসাহেবের নতুন বন্দরের কথা একদিন কানে এল পিডিংটনের। ওঁর কিন্তু এতটুকু সময় লাগল না বুঝতে যে কী মত্ততা লুকিয়ে আছে এই নদীর মধ্যে। এই মাতলার পাড়ে দাঁড়িয়ে তাকে উদ্দেশ্য করে সাহেব বললেন, “ওই সার্ভেয়ারদের তুমি কঁকি দিতে পার, কিন্তু আমার সঙ্গে তোমার ওসব চালাকি খাটবে না। তোমার কী ধান্দা তা আমার জানতে কিছু বাকি নেই। বাকিরাও যাতে জানতে পারে সে ব্যবস্থাও আমি শিগগিরই করছি।”
মনে মনে হাসল মাতলা। বলল, “যাও না, এক্ষুনি যাও। বলো না গিয়ে। তোমাকেই সবাই বলবে মাতলা–বলবে লোকটা নাকি নদী আর ঝড়ের মনের কথা পড়তে পারে।”
কলকাতায় নিজের বাড়িতে বসে একের পর এক চিঠি লিখতে লাগলেন পিডিংটন। প্ল্যানারদের লিখলেন, সার্ভেয়ারদের লিখলেন–কী বিপজ্জনক কাজ তারা করছে বললেন সে কথা; বললেন ভাটির দেশের এত গভীরে শহর গড়ার চিন্তা নিছক পাগলামি বই কিছু নয়; বাদাবন হল সাগরের সঙ্গে লড়ার জন্য বাংলার অস্ত্র, প্রকৃতির প্রচণ্ড আক্রমণ থেকে, দক্ষিণ বাংলাকে আড়াল করে রাখে এই জঙ্গল; ঝড়, ঢেউ, আর জলোচ্ছ্বাসের প্রথম ঝাঁপটাটা এই সুন্দরবনই সামলায়। ভাটির দেশ যদি না থাকত কবে জলের তলায় চলে যেত বাংলার সমতলক্ষেত্র: এই বাদাবনই তো এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছে পশ্চাভূমিকে। কলকাতার দীর্ঘ আঁকাবাঁকা সমুদ্রসড়ক আসলে হল সাগরের তুমুল শক্তির হাত থেকে বাঁচার জন্য প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। সেই তুলনায় তো এই নতুন বন্দর ভয়ানক অরক্ষিত। কখনও যদি সেরকম জোরালো স্রোত আর হাওয়ার টান ওঠে তা হলে সামান্য একটা ঝড়েই ভেসে যাবে গোটা জায়গাটা–সাইক্লোনের টানে একটা ঢেউ ওঠার শুধু অপেক্ষা। মরিয়া হয়ে পিডিংটন ভাইসরয়কে পর্যন্ত লিখে ফেললেন একটা চিঠি: বিষয়টা আরেকবার ভাল করে ভেবে দেখতে অনুরোধ করলেন, ভবিষ্যদ্বাণীও করলেন–বললেন, সত্যি সত্যি যদি বন্দর তৈরি হয় এই জায়গায়, পনেরো বছরের বেশি সে বন্দর টিকবে না। একদিন আসবে, যখন প্রচণ্ড সাইক্লোনের সঙ্গে আছড়ে পড়বে লোনা জলের বিশাল ঢেউ, ডুবিয়ে দেবে গোটা বসতিটাকে; এর জন্য মানুষ হিসাবে এবং বৈজ্ঞানিক হিসাবে নিজের মানসম্মান পণ রাখতেও তিনি রাজি–লিখলেন পিডিংটন।
খ্যাপা সাহেবের এসব কথায় অবশ্য কেউই কান দিল না; প্ল্যানারদের বা লাটসাহেবের কারওরই এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো সময় ছিল না। কে পিডিংটন? সামান্য একটা শিপিং ইন্সপেক্টর বই তো কেউ নয়। সাহেবদের জাতপাতের হিসেবে একেবারে নীচের দিকে তার স্থান। লোকে ফিসফাস করতে শুরু করল–আসলে মানুষটা একটু খ্যাপাটে তো, মাথায় অল্পবিস্তর গণ্ডগোল থাকাও বিচিত্র নয়। ও-ই তো কিছুদিন আগে বলেছিল না, যে ঝড় হল গিয়ে আসলে এক রকমের ‘আশ্চর্য ধূমকেতু’?
সুতরাং কাজ চলতেই থাকল, বন্দরও তৈরি হয়ে গেল। বাঁধানো রাস্তাঘাট হল, রং-টং করা তকতকে সব হোটেল ঘরবাড়ি হল, মোটকথা যেমন যেমন ভাবা হয়েছিল ঠিক সেইভাবে বানানো হল শহরটাকে। তারপর একদিন খুব হইহল্লা করে ঢাকঢোল বাজিয়ে উৎসব হল, ভাইসরয় পা রাখলেন মাতলার পাড়ে, নতুন বন্দরের নাম দিলেন পোর্ট ক্যানিং।
পিডিংটন সাহেবকে কিন্তু সে উৎসবে যোগ দিতে ডাকা হয়নি। কলকাতার রাস্তায় তাকে দেখা গেলেই এখন লোকজন হাসি তামাশা করে: ওই যে, ওই দেখ রে, মাতাল পিডিংটন বুড়ো যাচ্ছে। ওই লোকটাই তো নতুন বন্দরের কাজ আটকানোর জন্য জ্বালিয়ে মারছিল লাটসাহেবকে। কী একটা যেন ভবিষ্যদ্বাণীও করেছিল না? আবার নাকি মানসম্মান পণ রেখেছিল নিজের?
অপেক্ষা করো, অপেক্ষা করো, বললেন পিডিংটন–পনেরো বছর সময় দিয়েছি আমি। মাতাল সাহেবের ওপর দয়া হল মাতলার। পনেরো বছর তো অনেক লম্বা সময়, এর মধ্যেই যথেষ্ট ভোগান্তি হয়েছে লোকটার। একটা বছর সাহেবকে অপেক্ষা করিয়ে রাখল মাতলা, তারপর আরও এক বছর, তারপর আরও এক। এই করে করে কেটে গেল পাঁচ পাঁচটা বছর। অবশেষে একদিন, ১৮৬৭ সালে, যেন শক্তিপরীক্ষার সমস্ত প্রস্তুতি নিয়ে ফুঁসে উঠল নদী। আছড়ে পড়ল ক্যানিং-এর ওপর। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ভেসে গেল শহরটা–কঙ্কালটুকু শুধু পড়ে রইল।
বিশাল কোনও তুফান নয়, পিডিংটন ঠিক যেমনটি বলেছিলেন, সেইরকম সাধারণ একটা ঝড় উঠেছিল। সেই ঝড়ের হাওয়ায় নয়, তার সঙ্গে ওঠা একটা ঢেউয়ে একটা জলোচ্ছ্বাসে–গুঁড়িয়ে গেল গোটা শহর। তার চার বছর পর, ১৮৭১ সালে, অবশেষে পরিত্যক্ত বলে ঘোষণা করা হল বন্দরটাকে। যে বন্দরের একদিন পুব সাগরের রানি হয়ে ওঠার কথা ছিল, টক্কর দেওয়ার কথা ছিল বোম্বাই, সিঙ্গাপুর আর হংকং-এর সঙ্গে, সে এখন হয়ে গেল মাতলার কেনা বাঁদী–ক্যানিং।”
.
“মেশোর সব গল্পেরই শেষটা কিন্তু সবসময় রাখা থাকত সেই রিলকের জন্য,”কানাই বলল। বুকের ওপর হাত রেখে আবৃত্তি করতে লাগল:
‘তবু, হায়, কী-অদ্ভুত আর্তিপুরে জনপদগুলি…
আহা, দেবদূত, তিনি কেমন পায়ের তলে ধ্বস্ত করে দেবেন ওদের
সান্ত্বনা বাজার, যার এক পাশে তৈরি করা গির্জেটি নগদ মূল্যে
ক্রীত হয়ে, পড়ে আছে হতাশ ও পরিচ্ছন্ন–রুদ্ধ, যেন রবিবারে পোস্টাপিস।’
“বুঝতেই পারছেন ব্যাপারটা,” বলল কানাই। পিয়া ততক্ষণে হাসতে শুরু করেছে। “সেই ১৮৬৭ সালে মাতলা যেদিন লাটসাহেবের সাধের স্বপ্নকে গুঁড়িয়ে দিল, তারপর থেকে এভাবেই রয়ে গেছে ক্যানিং–রবিবারের ডাকঘরের মতো।”
.
একটি হত্যা
মেঘার কেবিনগুলোর প্রত্যেকটার মধ্যেই একটা করে উঁচু প্ল্যাটফর্ম মতো জায়গা আছে, বাঙ্ক হিসাবে ব্যবহার করার জন্য। সেখানে কম্বল চাদর আর বালিশ পেতে একটা বিছানা বানিয়ে নিয়েছিল কানাই। খুব একটা শৌখিন কিছু না, তবে মোটামুটি আরামদায়ক। তার ওপরে শুয়ে বেশ ভালই ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ লোকজনের গলার আওয়াজে ঘুমটা ভেঙে গেল। মনে হল চারিদিকে অনেক লোকের হইচই। কিছু আওয়াজ দূর থেকে ভেসে আসছে, কিছু কাছ থেকে। হাতড়ে টর্চটা নিয়ে ঘড়ি দেখল কানাই–রাত তিনটে। ওপরের ডেক থেকে হরেন আর তার নাতির গলা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে, দুজনেই মনে হল খুব উত্তেজিত।
ঘুমোতে যাওয়ার আগে জামাকাপড় ছেড়ে শুধু একটা লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরে নিয়েছিল কানাই, এখন গা থেকে কম্বলটা সরাতেই হাওয়ার ঠান্ডা ভাবটা টের পেল বেশ। কেবিন থেকে বেরোনোর আগে একটা কম্বল তুলে পেঁচিয়ে নিল গায়ে। হরেন আর তার নাতি কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, রেলিং-এর ওপর ঝুঁকে পড়ে তাকিয়ে ছিল পাড়ের দিকে।
“কী হয়েছে?” কানাই জিজ্ঞেস করল।
“ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। গায়ে কিছু একটা হয়েছে মনে হচ্ছে।”
মাঝনদীতে নোঙর করা রয়েছে বোটটা। বেশ কয়েক ঘণ্টা আগে জোয়ারও লেগে গেছে; পাড় থেকে ওদের দূরত্ব এখন কম করে এক কিলোমিটার। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তুলো তুলো মেঘের মতো হিম উঠে এসেছে জলের বুক থেকে: ভোরের কুয়াশার মতো ঘন না হলেও দূরের পাড়ি অনেকটা আবছা লাগছে তাতে। কাঁপা কাঁপা হিমের চাদরের মধ্যে দিয়ে দেখা গেল কয়েকটা কমলা রং-এর আলোর বিন্দু খুব তাড়াতাড়ি এদিক ওদিক নড়াচড়া করছে, যেন জ্বলন্ত মশাল নিয়ে পাড় বেয়ে দৌড়োদৌড়ি করছে কিছু লোক। কুয়াশা সত্ত্বেও এতটা দূর থেকে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে তাদের গলার আওয়াজ। এতগুলি লোক এই মাঝরাত্তিরে কেন এভাবে ছুটোছুটি করছে সেটা হরেন আর তার নাতিও মনে হল ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।
হঠাৎ কনুইয়ে কার একটা ছোঁয়া পেল কানাই। ঘুরে তাকিয়ে দেখল পিয়া দাঁড়িয়ে আছে পাশে, চোখ ঘষছে হাত মুঠো করে। “কী হয়েছে?”
“সেটাই বোঝার চেষ্টা করছি। এরাও কেউ বলতে পারছে না।”
“ফকিরকে একবার জিজ্ঞেস করুন না।”
ভটভটির পেছন দিকটায় গেল কানাই, পিয়াও গেল সঙ্গে সঙ্গে। নীচে নৌকোর ওপর টর্চের আলো ফেলতে দেখা গেল জেগেই আছে ফকির, একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে নৌকোর মাঝখানটায় বসে আছে জড়োসড়ো হয়ে। মুখে আলো পড়তে হাত তুলে চোখ আড়াল করল। টর্চটা নিভিয়ে দিল কানাই। একটু ঝুঁকে পড়ে কী কথা বলল ফকিরের সঙ্গে।
“ও জানে কী হয়েছে?” পিয়া জানতে চাইল।
“না। ডিঙি নিয়ে যাবে বলছে পাড়ে। বলছে চাইলে আমরাও যেতে পারি ওর সঙ্গে।”
“সে তো যাবই।”
ফকিরের নৌকোয় চড়ে বসল কানাই আর পিয়া। নাতিকে ভটভটিটার দায়িত্বে রেখে হরেনও চলে এল ওদের সঙ্গে।
পাড় পর্যন্ত যেতে প্রায় মিনিট পনেরো লাগল। এগোতে এগোতেই বোঝা যাচ্ছিল, একটা নির্দিষ্ট জায়গাকে কেন্দ্র করে হল্লাটা হচ্ছে: মনে হল হরেনের আত্মীয়রা গ্রামের যে জায়গাটায় থাকে ঠিক সেইখানটাতেই এসে জড়ো হচ্ছে সব লোকজন। ডাঙা যত কাছে আসতে থাকল ততই জোর হতে লাগল লোকের কথাবার্তা আর চিৎকার চেঁচামেচি, বাড়তে বাড়তে একসময় সমস্ত আওয়াজ মিশে গিয়ে শুধু ক্রুদ্ধ ধকধকে একটা শব্দে পরিণত হল।
আওয়াজটা শুনতে শুনতে কেমন একটা ভয় ধরে গেল কানাইয়ের। হঠাৎ একটা ঝোঁকের মাথায় বলল, “পিয়া, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আমাদের আর এগোনোটা উচিত হবে কিনা।”
“কেন?”
“এই হইচই-টা শুনে আমার কী মনে হচ্ছে জানেন?” কানাই জিজ্ঞেস করল।
“কী, একটা জটলা-টটলা কিছু?”
“জটলা ঠিক নয়, বলা যেতে পারে ‘মব’–উত্তেজিত জনতা।”
“মব? এইটুকু একটা গ্রামে মব?”
“ব্যাপারটা বিশ্বাস করা কঠিন, তবে আওয়াজ যা শোনা যাচ্ছে তাতে আমার মনে হচ্ছে বড় ধরনের কোনও দাঙ্গা-হাঙ্গামা হচ্ছে ওখানে, আর দাঙ্গা আমি সামনাসামনি দেখেছি, চোখের সামনে লোক মরতেও দেখেছি। আমার মন বলছে সেইরকমই কিছু একটা হাঙ্গামার মধ্যে গিয়ে পড়তে চলেছি আমরা।”
চোখের ওপর হাত আড়াল করে কুয়াশার মধ্যে দিয়ে গ্রামটার দিকে দেখতে লাগল পিয়া। “ব্যাপারটা দেখাই যাক না গিয়ে।”
জোয়ার শেষ হয়ে ভাটা পড়ে গেছে বেশ কিছুক্ষণ হল, কিন্তু নদী এখনও টইটম্বুর। খুব সহজেই ফকির ডিঙির গলুইটা পাড়ের কাদার মধ্যে নিয়ে তুলল। সামনে থেকে উঠে গেছে ভেজা মাটির ঢাল, বাদাবনের অন্ধকারে ঢাকা, তাদের শ্বাসমূল আর ছোট ছোট চারায় ভর্তি চারদিক। ভিড়টা যেখানে জড়ো হয়েছে তার কাছাকাছি নৌকোটা নিয়ে গিয়ে ভিড়িয়েছে। ফকির, ডিঙি থেকে সামনে ছায়ার মতো দেখা যাচ্ছে বাঁধটা, তার ওপর জমাট কুয়াশা–লালচে আভা ধরেছে মশালের আলোয়।
কানাই আর পিয়া বনবাদাড়ের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে এগোচ্ছিল সামনের দিকে, হাত নেড়ে ওদের থামিয়ে দিল হরেন। কানাইয়ের হাত থেকে টর্চটা নিয়ে পায়ের কাছে মাটিতে একটা জায়গায় আলো ফেলল। কাছে গিয়ে কানাই আর পিয়া দেখল মাটির মধ্যে একটা দাগের ওপর গিয়ে পড়েছে আলোটা। মাটিটা এখানে একটু নরম, ঠিক ভেজাও নয়, আবার শুকনোও নয়। তার ওপর স্পষ্ট হয়ে বসে গেছে ছাপটা, স্টেনসিলে আঁকা ছবির মতো। ওটা কীসের দাগ সেটা বুঝতে একটুও সময় লাগল না কানাইয়ের আর পিয়ার। রান্নাঘরের মেঝেতে বেড়ালের পায়ের ছোপ যেরকম দেখতে লাগে, এই দাগটাও খানিকটা সেইরকম–শুধু তার চেয়ে বহুগুণ বড়। এত স্পষ্টভাবে ছাপটা পড়েছে যে তার মধ্যে থাবার গোলগোল মাংসল অংশের গড়ন আর গুটিয়ে নেওয়া নখের দাগ আলাদা করে দেখা যাচ্ছিল। টর্চের আলোটা সামনের দিকে ফেলল হরেন। হুবহু একরকম ছাপ পরপর নদীর পাড় থেকে সোজা চলে গেছে বাঁধের ওপর। দাগগুলো দেখে জানোয়ারটা কোন পথে এসেছে তার একটা আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছিল। ওপারের জঙ্গল থেকে নেমে সাঁতরে নদী পার হয়েছে, আর এদিকে এসে পাড়ে যেখানটায় উঠেছে, ঠিক সেই জায়গাটাতেই এখন ভাসছে ফকিরের নৌকো।
“যেখান দিয়ে ওটা নদী পেরিয়েছে সেই জায়গাটা মেঘার থেকে নিশ্চয়ই দেখা যাচ্ছিল,” পিয়া বলল।
“খুব সম্ভবত। কিন্তু আমরা সবাই যেহেতু ঘুমিয়ে ছিলাম তাই কেউ দেখে ফেলার ভয়টা মনে হয় ছিল না ওর।”
বাঁধের মাথার কাছাকাছি পৌঁছে মাটিতে বড়সড় একটা ছাপের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল হরেন। ইশারায় বলল এখানে বসেই গ্রামটাকে পর্যবেক্ষণ করে ওর শিকার বেছে নিয়েছিল জানোয়ারটা। মাটিতে আরেকটা দাগের দিকে দেখিয়ে বলল খুব সম্ভবত এখান থেকেই লাফ দিয়ে পড়েছিল শিকারের ওপর। বলতে বলতে উদ্বেগে অধীর হয়ে সামনের দিকে ছুটতে শুরু করল বুড়ো মানুষটা। ফকিরও দৌড়ল সঙ্গে সঙ্গে। কয়েক পা পেছনেই চলল পিয়া আর কানাই। কিন্তু বাঁধের ওপরে পৌঁছতেই যে দৃশ্য চোখে পড়ল তাতে সবাই থমকে থেমে গেল একসঙ্গে। মশালের আলোয় দেখা যাচ্ছিল গোটা গ্রামটা গায়ে গায়ে লাগা কতগুলি মাটির বাড়ির জটলার মতো। বাঁধের সমান্তরাল ভাবে পরপর চলে গেছে বাড়িগুলো। ওদের ঠিক সামনে, শখানেক মিটার দূরে, দেখা যাচ্ছিল একটা মাটির দেওয়ালওয়ালা ঘর, খোড়ো ছাউনি দেওয়া। কুঁড়েটার চারদিকে ঘিরে প্রায় একশো লোক জড়ো হয়েছে। বেশিরভাগই পুরুষমানুষ, তাদের অনেকের হাতে লম্বা বাঁশের বল্লম, সামনের দিকটা চেঁছে ছুঁচোলো করা। সেই বল্লমগুলো ওরা বারবার গেঁথে দিচ্ছে মাটির ঘরটার মধ্যে। প্রচণ্ড ভয় আর ক্রোধে বিকৃত হয়ে গেছে লোকগুলোর মুখ। ভিড়ের মধ্যে যে ক’জন মহিলা আর বাচ্চা আছে সমস্বরে তারা চিৎকার করছে:
“মার! মার!”
ভিড়টার একধারে হরেনকে দেখতে পেয়ে কানাই আর পিয়া সেদিকে এগিয়ে গেল। “এখানেই আপনার আত্মীয়রা থাকেন?” জিজ্ঞেস করল কানাই।
“হ্যাঁ,” বলল হরেন। “এখানেই থাকে ওরা।”
“কী হয়েছে? গণ্ডগোলটা কীসের?”
“সেই যে মোষের বাচ্চা হওয়ার আওয়াজ শুনেছিলাম আমরা মনে আছে?” হরেন বলল।
“সেই থেকেই শুরু হয়েছে ব্যাপারটা। নদীর ওপার থেকে বড়মিঞাও শুনেছে আওয়াজটা। তারপর জল পেরিয়ে চলে এসেছে এদিকে।”
সামনের কুঁড়েটা আসলে একটা গোয়ালঘর, বলল হরেন। কাছেই একটু বড় আরেকটা কুঁড়েতে থাকে ওর আত্মীয়রা। আধঘণ্টাখানেক আগে হঠাৎ হুড়মুড় করে একটা শব্দ আর গোরুমোষের চিৎকারে ওদের ঘুম ভেঙে যায়। বাইরে তখন ঘন অন্ধকার। কুয়াশাও ছিল বেশ। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে তাই কিছুই দেখতে পায়নি ওরা, কিন্তু যেটুকু শুনতে পেয়েছে তাতেই পরিষ্কার বোঝা গেছে কী ঘটেছে ব্যাপারটা: বড় একটা জানোয়ার লাফ দিয়ে এসে পড়েছে গোয়ালঘরটার ওপর, আর নখ দিয়ে খড়ের চালে গর্ত করার চেষ্টা করছে। একটু পরেই আরেকটা ধড়মড় করে আওয়াজে বোঝা গেছে জানোয়ারটা ঢুকে পড়েছে গোয়ালের ভেতরে। বাড়িতে ছয় ছয়টা জোয়ান লোক। ওরা দেখল এরকম সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। বাঘটা এ গাঁয়ে নতুন নয়, আগেও এসেছে বেশ কয়েকবার। দু’বার দুটো লোককে মেরেছে, গোরু-ছাগলও খেয়েছে অনেকগুলো। এখন গোয়ালঘরের মধ্যে ওটা যতটুকু সময় আছে তার মধ্যে ওকে কবজা করা খুব একটা কঠিন হবে না। কারণ ওখান থেকে পালাতে হলে ওকে খাড়া লাফ দিয়ে চালের ওই ঘেঁদাটার মধ্যে দিয়ে বেরোতে হবে। একটা বাঘের পক্ষেও সেটা খুব একটা সোজা কাজ নয়। আর মুখে একটা বাছুর নিয়ে ওভাবে লাফিয়ে বেরোনো তো আরও কঠিন।
বাড়িতে যে ক’টা মাছ-ধরা জাল ছিল সবগুলো নিয়ে ওরা বেরিয়ে এল। একটার পর একটা সেগুলোকে ছুঁড়ে দিল গোয়ালঘরের চালের ওপর। তারপর কাঁকড়া ধরার নাইলন দড়ি দিয়ে শক্ত করে একসঙ্গে বাঁধল জালগুলোকে। এবার বাঘটা বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য যেই লাফ দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে গেছে জালে; আর ফের গিয়ে পড়েছে গোয়ালঘরের ভেতর। বেরোনোর জন্য ছটফট করছে ওটা তখন। সেই সময় ছেলেদের মধ্যে একজন একটা বাঁশের বল্লম জানালা দিয়ে সোজা ঢুকিয়ে দিয়েছে ওর চোখের মধ্যে।
হরেন যেমন যেমন বলে যাচ্ছিল, সঙ্গে সঙ্গে কথাগুলি ইংরেজিতে অনুবাদ করে যাচ্ছিল কানাই পিয়ার জন্য। কিন্তু এই পর্যন্ত শুনেই ওকে থামিয়ে দিল পিয়া। কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, “তার মানে আপনি বলতে চাইছেন বাঘটা এখনও এই চালাঘরটার মধ্যে রয়েছে?”
“হ্যাঁ,” বলল কানাই। “এখানেই আটকে রয়েছে বাঘটা এখন, অন্ধ অবস্থায়।”
পিয়া একবার মাথাটা ঝাঁকাল, যেন একটা দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে ওঠার চেষ্টা করছে। দুর্বোধ্য একটা দৃশ্য ঘটে যাচ্ছে চোখের সামনে, কিন্তু তার প্রতিটা খুঁটিনাটি এত স্পষ্ট, যে এতক্ষণে পিয়া বুঝতে পারল এই সব তীক্ষ্ণ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এতগুলি লোক আসলে ওই আহত প্রাণীটাকে আক্রমণ করছে। পুরো ব্যাপারটা তখনও ও বোঝার চেষ্টা করছে, এমন সময় সাড়া দিল বাঘটা, এই প্রথম বার। মুহূর্তের মধ্যে গোয়ালঘরের থেকে দূরে সরে গেল লোকজন। বল্লম-উল্লম ফেলে হাত দিয়ে মুখ আড়াল করল সবাই, যেন প্রচণ্ড কোনও বিস্ফোরণ থেকে বাঁচার চেষ্টা করছে। এমন তীব্রতা সে আওয়াজের যে পায়ের নীচের মাটি পর্যন্ত কেঁপে কেঁপে উঠছিল তাতে, নিজের খালি পায়ের চেটোয় সেটা স্পষ্ট অনুভব করল পিয়া। এক মুহূর্তের জন্য সকলের সব নড়াচড়া থেমে গেল। তারপর যেই পরিষ্কার হল যে বাঘটা এখনও গোয়ালঘরের মধ্যেই অসহায় বন্দি অবস্থাতেই রয়েছে, অমনি বল্লম তুলে নিয়ে দ্বিগুণ ক্রোধে সেদিকে তেড়ে গেল সবাই।
কানাইয়ের হাতটা খামচে ধরে ওর কানের কাছে চিৎকার করে পিয়া বলল, “এক্ষুনি কিছু একটা করতে হবে, কানাই। এটা কিছুতেই হতে দেওয়া যায় না।”
“কিছু করতে পারলে ভাল হত পিয়া, কিন্তু উপায় কিছু আছে বলে তো মনে হচ্ছে না।”
“কিন্তু একটা চেষ্টা তো করে দেখা যেতে পারে, কানাই, করা যায় না কিছু?” পিয়ার গলায় অনুনয়ের সুর।
এর মধ্যে হরেন এসে ফিসফিস করে কী যেন বলল কানাইয়ের কানে কানে। সঙ্গে সঙ্গে পিয়ার হাতটা ধরে বাঁধের দিকে ফেরানোর চেষ্টা করল কানাই। “শুনুন পিয়া, আমাদের ফিরে যেতে হবে এখন।”
“ফিরে যেতে হবে? কোথায়?”
“লঞ্চে ফিরতে হবে,” কানাই বলল।
“কেন?” জিজ্ঞেস করল পিয়া। “কী হবে এখন এখানে?”
পিয়ার হাতটা ধরে টানতে শুরু করল কানাই। “যাই হোক না কেন, এখানে দাঁড়িয়ে সেটা না দেখাই ভাল আপনার।”
মশালের আলোয় উজ্জ্বল ওর মুখের দিকে তাকাল পিয়া। “কী লুকোচ্ছেন আপনি আমার থেকে? কী করতে চাইছে এরা?”
মাটিতে থুতু ফেলল কানাই। একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করুন পিয়া–এই জানোয়ারটা বহুদিন ধরে বার বার এ গ্রামে হানা দিচ্ছে। দু-দুটো লোককে মেরেছে, গোরু-ছাগল যে কত মেরেছে তার ইয়ত্তা নেই–”
“কিন্তু ওটা তো জানোয়ার, কানাই,” বলল পিয়া। “জানোয়ারের ওপর আপনি প্রতিশোধ নিতে পারেন না।”
চারিদিকে উন্মত্তের মতো চিৎকার করছে গ্রামের লোকেরা, মশালের দপদপে আলোয় চকচক করছে তাদের মুখগুলো: মার! মার! পিয়ার কনুইটা ধরে ওকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল কানাই। “দেরি হয়ে গেছে পিয়া, আর কিছু করার নেই। আমাদের চলে যেতে হবে এখন।”
“চলে যাব?” পিয়ার গলায় বিস্ময়। “কিছুতেই যাব না আমি। আমি এটা আটকাব।”
“পিয়া, এটা একটা উন্মত্ত মব, খেপে গেলে আমাদেরও অ্যাটাক করতে পারে ওরা। আমরা এখানে বাইরের লোক।”
“তা হলে শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবেন?”
“আমাদের পক্ষে এখানে কিছু করা সম্ভব নয় পিয়া,” প্রায় চিৎকার করে বলল কানাই। “ঠান্ডা মাথায় একটু বোঝার চেষ্টা করুন ব্যাপারটা। চলুন, চলে যাই এখান থেকে।”
এক ঝাঁকুনি দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিল পিয়া। “আপনি যেতে চান তো চলে যান, কিন্তু আমি কিছুতেই এভাবে কাপুরুষের মতো পালাব না। আপনি যদি কিছু না করেন, তা হলে আমি করব। আর ফকির–আমি জানি ফকিরও করবে। ও কোথায় গেল?”
আঙুল তুলে দেখাল কানাই। “ওখানে। দেখুন।”
বুড়ো আঙুলের ওপর ভর দিয়ে ডিঙি মেরে পিয়া দেখল ভিড়টার একেবারে সামনের দিকে দেখা যাচ্ছে ফকিরকে, একটা বাঁশের বল্লম চেঁছে ছুঁচোলো করে দিচ্ছে একজনকে। এক ধাক্কায় কানাইকে সরিয়ে দিয়ে ভিড়টার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল পিয়া। ঠেলতে ঠেলতে চলে গেল ফকিরের কাছ পর্যন্ত। সঙ্গে সঙ্গে ওদের চারপাশের ভিড়টা বেড়ে উঠল, মানুষের চাপে ফকিরের পাশের লোকটার গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে গিয়ে পড়ল পিয়া। মশালের দপদপে আলোয় কাছ থেকে বল্লমটা দেখতে পেল পিয়া। ছুঁচোলো ডগাটায় রক্তের দাগ। আর বাঁশের চেঁাচের ফাঁকে ফাঁকে লেগে আছে কয়েকগুছি হলদে কালো লোম। হঠাৎ পিয়ার মনে হল ও যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে জানোয়ারটাকে–ভয়ে গুটিসুটি মেরে এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে গোয়ালঘরটার ভেতরে, সরে সরে গিয়ে ছুঁচোলো বল্লমগুলোর থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করছে, গায়ের জায়গায় জায়গায় গর্ত হয়ে গেছে মাংসের মধ্যে, সেই ক্ষতস্থানগুলি চাটছে। হাত বাড়িয়ে একটানে বল্লমটা কেড়ে নিল ও, সামনের লোকটার কাছ থেকে। তারপর পায়ের চাপে সেটাকে ভেঙে ফেলল দু’টুকরো করে।
এক মুহূর্তের জন্য ভীষণ হতভম্ব হয়ে গেল লোকটা। তারপর হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করে কী সব বলতে লাগল আর একটা হাত মুঠো করে ঝাঁকাতে থাকল পিয়ার মুখের সামনে। মিনিট খানেকের মধ্যে আরও জনা ছয়েক এসে জুটে গেল লোকটার সঙ্গে। বয়স কারওরই খুব একটা বেশি নয়, মাথায় একটা করে চাদর জড়ানো সবার। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কী যে বলতে লাগল একবর্ণও তার বুঝল না পিয়া। এমন সময় কার একটা হাত এসে ধরল ওর কনুইটা। ফিরে তাকিয়ে দেখল ফকির দাঁড়িয়ে রয়েছে ওর পেছনে। ওকে দেখে ভরসা পেল পিয়া: আশায় আর স্বস্তিতে হঠাৎ যেন অবশ হয়ে গেল মনটা। মনে হল ফকির ঠিক জানবে কী করতে হবে, এই সব পাগলামি বন্ধ করার কিছু একটা উপায় ঠিক ও বের করবে। কিন্তু সেসব কিছু করার বদলে ফকির এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল ওকে, বুকের সঙ্গে চেপে ধরে সরিয়ে নিয়ে চলল ভিড় ঠেলে। দু’পায়ে ওর হাঁটুতে লাথি মারতে লাগল পিয়া, খামচে দিল হাতদুটো। তার মধ্যেই হঠাৎ দেখতে পেল ভিড়টার মধ্যে থেকে একটা আগুনের গোলা উড়ে গিয়ে পড়ল গোয়ালঘরটার ওপর। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চালাটার ওপর গজিয়ে উঠতে শুরু করল লকলকে আগুনের শিখা। আরেকবার শোনা গেল গর্জন। তার এক মুহূর্ত পর ভিড়টা থেকে জবাব এল সে গর্জনের, উন্মত্ত রক্তলোলুপ চিৎকার–মার! মার! গোয়ালের ওপর লাফিয়ে বাড়তে লাগল আগুন, কাঠকুটো আর শুকনো খড় দিয়ে সেটাকে আরও উশকে দিতে থাকল লোকজন।
ফকিরের হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল পিয়া। চিৎকার করতে শুরু করল: “ছাড়ো আমাকে ছেড়ে দাও!”
কিন্তু ছেড়ে দেওয়ার বদলে ওকে ঘুরিয়ে ধরল ফকির, চেপে ধরল নিজের শরীরের সঙ্গে; তারপর খানিকটা হেঁচড়ে, খানিকটা পাঁজাকোলা করে বাঁধের ওপর নিয়ে গিয়ে তুলল। লাফিয়ে বাড়তে থাকা আগুনের আলোয় পিয়া দেখল কানাই আর হরেন সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চারপাশ থেকে ঘিরে ওকে বাঁধ থেকে নামিয়ে নৌকোর দিকে নিয়ে চলল ওরা।
বাঁধের গা বেয়ে হোঁচট খেতে খেতে নামতে নামতে কোনওরকমে নিজেকে সংযত করে খুব ঠান্ডা গলায় পিয়া শুধু বলতে পারল, “ফকির, আমাকে ছেড়ে দাও। কানাই, ওকে বলুন আমাকে ছেড়ে দিতে।”
হাতটা একটু আলগা করল ফকির, কিন্তু অনিচ্ছার সঙ্গে। পিয়া একটু সরে দাঁড়াতেই প্রায় লাফ দিয়ে উঠল ও, মনে হল গ্রামের দিকে ফের দৌড়তে চেষ্টা করলেই গিয়ে ধরে ফেলবে আবার।
বাঁধের এপার থেকে ধু ধু করে জ্বলা আগুনের শব্দ কানে আসছিল পিয়ার, হাওয়ায় ভেসে আসছিল পোড়া চামড়া আর মাংসের গন্ধ। ওর কানের কাছে মুখ এনে কী যেন একটা বলল ফকির। কানাইয়ের দিকে ফিরে পিয়া জিজ্ঞেস করল, “কী বলল ও?”
“ও আপনাকে এতটা আপসেট হতে বারণ করছে।”
“আপসেট হব না? কী বলছেন আপনি? এরকম ভয়ংকর ব্যাপার আমি জীবনে দেখিনি–জ্যান্ত একটা বাঘকে পুড়িয়ে মেরে ফেলল?”
“ও বলছে বাঘ যখন গ্রামে আসে তখন মরতে চায় বলেই আসে।”
হাত দিয়ে দু’কান চেপে ফকিরের দিকে ফিরল পিয়া, “স্টপ ইট। এই নিয়ে আর কোনও কথা আমি শুনতে চাই না। লেটস জাস্ট গো।”
.
জেরা
পিয়ারা যখন বোটে গিয়ে উঠল ততক্ষণে ভোর হয়ে এসেছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মেঘার নোঙর তুলে ইঞ্জিন চালু করে দিল হরেন। বলল, যত তাড়াতাড়ি এখান থেকে সরে পড়া যায় ততই মঙ্গল। বাঘ মারার খবর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কানে পৌঁছলেই সঙ্গে সঙ্গে ঝামেলা শুরু হয়ে যাবে। তারপর দাঙ্গা, গোলাগুলি, পাইকারি হারে গ্রেফতার–সবই হতে পারে। সেরকম অভিজ্ঞতা আগে হয়েছে হরেনের।
ভটভটির মুখ ঘুরতে শুরু করতেই জামাকাপড় পালটানোর জন্য নিজের কেবিনের দিকে চলল কানাই। আর পিয়া, খানিকটা যেন অভ্যাসের বশে, ওপরের ডেকের সামনে ওর নিজের জায়গার দিকে এগিয়ে গেল। কানাইয়ের মনে হল কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওর ‘নজরদারি’ ফের চালু হয়ে যাবে। কিন্তু কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে কানাই দেখল ডেকের ওপর কেমন যেন গা ছেড়ে দিয়ে বসে আছে পিয়া, মাথাটা হতাশ ভাবে রেলিঙের ওপর হেলানো। ভঙ্গিটা দেখে কানাই পরিষ্কার বুঝতে পারল এতক্ষণ এখানে বসে বসে কাঁদছিল পিয়া।
ওর পাশে গিয়ে বসল কানাই। বলল, “মিছিমিছি এভাবে কষ্ট পাওয়ার কোনও মানে হয় পিয়া। ওখানে আমাদের কিছুই করার ছিল না।”
“একবার চেষ্টা তো করতে পারতাম।”
“তাতে লাভ কিছুই হত না।”
“হয়তো হত না,” হাতের পেছন দিয়ে চোখ মুছল পিয়া। “যাক গে। তবে আপনার কাছে মনে হয় একটা ব্যাপারে আমার ক্ষমা চাওয়ার আছে কানাই।”
“ওখানে যা সব বলেছিলেন সে জন্য?” হাসল কানাই। “তাতে কিছু মনে করিনি আমি– আপনার রাগ করার যথেষ্ট সংগত কারণ ছিল।”
মাথা নাড়ল পিয়া, “না–শুধু সে জন্যে নয়।”
“তা হলে?”
“গতকাল আপনি আমাকে কী বলছিলেন মনে আছে?” জিজ্ঞেস করল পিয়া। “ঠিকই বলেছিলেন আপনি। আমিই আসলে ভুল বুঝেছিলাম।”
“আমি ঠিক বুঝতে পারছি না–কোন ব্যাপারে কথা বলছেন আপনি,” কানাই বলল। “ওই যে আপনি বলছিলেন না–সেই যে, কোনও রকমের কোনও মিলই নেই..”
“আপনার আর ফকিরের মধ্যে?”
“হ্যাঁ,” বলল পিয়া। “ঠিকই বলেছিলেন আপনি। আমিই আসলে বোকামি করছিলাম। মনে হয় এরকম কিছুর একটা দরকার ছিল আমার ভুলটা ভাঙার জন্য।”
জয়ের আনন্দে প্রথমেই যে কথাটা মুখে আসছিল একটু চেষ্টা করে সেটা গিলে ফেলল কানাই। গলার স্বর যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রেখে জিজ্ঞেস করল, “এই গভীর উপলব্ধি আপনার কীভাবে হল সেটা জানা যেতে পারে কি?”
“এইমাত্র যা ঘটে গেল তার থেকেই হল,” বলল পিয়া। “ফকিরের এইরকম ব্যবহার আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না।”
“কিন্তু এ ছাড়া আর কী আশা করেছিলেন ওর কাছ থেকে আপনি, পিয়া?” কানাই জিজ্ঞেস করল। “আপনি কি ভেবেছিলেন ও আসলে মাটির থেকে উঠে আসা একজন পরিবেশবিদ? তাও নয়। ফকির একজন জেলে পেটের জন্য মাছ মারাই ওর কাজ।”
“সেটা বুঝতে পারি,” পিয়া বলল। “ওকে দোষ দিচ্ছি না আমি। আমি জানি ছোটবেলা থেকে এই ভাবেই ও বেড়ে উঠেছে। আসলে আমি ভেবেছিলাম ও হয়তো ঠিক অন্য সকলের মতো নয়, একটু আলাদা।”
সহানুভূতির সঙ্গে পিয়ার হাটুতে আলতো করে হাত রাখল কানাই। “বাদ দিন এসব আলোচনা এখন। সামনে অনেক কাজ পড়ে আছে আপনার।”
মাথা তুলে তাকাল পিয়া। একটু চেষ্টার হাসি ফোঁটাল মুখে।
.
ঘণ্টাখানেকের পথ পেরিয়ে এসেছে মেঘা, এমন সময় ছাই-রঙা একটা মোটরবোট সশব্দে বেরিয়ে গেল পাশ দিয়ে। পিয়া তখন দূরবিন চোখে ভটভটির সামনে দাঁড়িয়ে, আর কানাই বসে আছে ছাউনির নীচে। দুজনেই তাড়াতাড়ি পাশের দিকটায় গিয়ে উঁকি মেরে দেখল তিরবেগে ভাটির দিকে চলে যাচ্ছে বোটটা, তাতে ভর্তি খাকি পোশাক পরা ফরেস্ট গার্ড। যে গ্রাম থেকে ওরা খানিক আগে এসেছে সেইদিকেই যাচ্ছে মনে হল।
এর মধ্যে হরেনও এসে দাঁড়িয়েছে ওদের পাশে। ও কিছু একটা বলল, তাতে হো হো করে হেসে উঠল কানাই। পিয়াকে ব্যাখ্যা করে বলল, “হরেন বলছে কারও যদি কখনও এরকম অবস্থা হয় যে একদিকে গেলে জলদস্যুর হাতে পড়বে আর অন্য দিকে গেলে ফরেস্ট গার্ডের হাতে, তা হলে জলদস্যুর দিকে যাওয়াটাই ভাল। কম বিপজ্জনক।”
কাষ্ঠ হেসে ঘাড় নাড়ল পিয়া। ফরেস্ট গার্ডদের সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ল ওর। জিজ্ঞেস করল, “ওরা কী করতে যাচ্ছে ওখানে?”
“ধরপাকড়, জরিমানা, মারধর–আরও কী কী করবে কে জানে,” কানাই বলল।
আরও ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। একটা মোহনা পার হতে গিয়ে বেশ কয়েকটা ছাই-রঙা মোটরবোটের একটা দল চোখে পড়ল ওদের। আগের বোটটা যেদিকে গেছে মনে হল এগুলোও সেই একই দিকে যাচ্ছে।
“আরেব্বাস,” বলে উঠল পিয়া। “এরা তো মনে হচ্ছে সহজে ছাড়বে না।”
“সেরকমই দেখা যাচ্ছে,” বলল কানাই।
হঠাৎ একটা মোটরবোট মুখ ঘুরিয়ে দল ছেড়ে বেরিয়ে এল। স্পিড বাড়াতে বোঝা গেল সোজা মেঘার দিকেই আসছে ওটা।
হরেনও দেখতে পেয়েছে বোটটাকে। সারেঙের ঘরের ভেতর থেকে মুখ বের করে ব্যস্ত ভাবে কী যেন একটা বলল কানাইকে।
“পিয়া, আপনাকে এবার কেবিনে ঢুকে পড়তে হবে,” কানাই বলল। “হরেন বলছে যদি আপনাকে ওরা লঞ্চে দেখতে পায় তা হলে ঝামেলা হতে পারে। মানে, আপনি বিদেশি আর ঠিকমতো পারমিট-টারমিট নেই, এসব বলে ঝাট করতে পারে।”
“ওকে।” পিঠব্যাগটা তুলে নিয়ে কেবিনে গিয়ে ঢুকল পিয়া। দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিল ভেতর থেকে। বাঙ্কে শুয়ে পড়ে ক্রমশ জোরালো হতে থাকা মোটরবোটের ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে লাগল। শব্দটা যখন থেমে গেল, ও বুঝতে পারল বোটটা মেঘার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তারপর শুনতে পেল লোকজনের কথাবার্তার আওয়াজ, বাংলায়। প্রথমটায় শান্ত ভদ্র সুরে কথা শুরু হল, তারপর সুর চড়তে আরম্ভ করল আস্তে আস্তে। অনেকের গলার মধ্যে থেকে কানাইয়ের গলাটা আলাদা করে শুনতে পেল পিয়া।
ঝাড়া একটা ঘণ্টা কেটে গেল এই করে। যুক্তি, পালটা যুক্তি চলতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে ওঠানামা করতে লাগল গলার স্বর। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গুমোট বাড়ছে কেবিনের ভেতর। ভাগ্যিস একটা জলের বোতল ছিল পিয়ার কাছে।
আরও বেশ খানিকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে থেমে গেল কথাবার্তার আওয়াজ। মোটরবোটটাও ফিরে চলে গেল তারপর। ধকধক শব্দ উঠল মেঘার ইঞ্জিনে, আর পিয়ার কেবিনের দরজায় কে এসে ঠকঠক আওয়াজ করল। দরজা খুলে কানাইকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল পিয়া।
“কী এত গোলমাল হচ্ছিল?”
মুখ বাঁকাল কানাই। “যা বোঝা গেল, ওরা শুনেছে কালকে যখন বাঘটাকে মারা হয়েছে তখন একজন বিদেশি ওই গ্রামে ছিল। তাই ওরা নাকি ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেছে।”
“কেন?”
“বলছে যে বর্ডারের এত কাছে গার্ড ছাড়া ঘুরে বেড়ানো নাকি একজন ফরেনারের পক্ষে খুব বিপজ্জনক। কিন্তু আমার মনে হয় ওরা আসলে খবরটা বাইরে ছড়াতে দিতে চায় না।”
“বাঘ মারার খবরটা?”
“হ্যাঁ,” মাথা নাড়ল কানাই। “এতে করে ওদের সম্পর্কে লোকের ধারণা খারাপ হয়ে যাবে। কিন্তু একটা জিনিস যেটা বোঝা যাচ্ছে সেটা হল আপনি যে এই এলাকায় ঘোরাফেরা করছেন সেটা ওরা জানে, আর এটাও পরিষ্কার যে আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে ওরা। বারবার জিজ্ঞেস করছিল আমরা আপনাকে দেখেছি কিনা।”
“কী বললেন আপনারা?”
হাসল কানাই। “হরেন আর আমি তো পুরো অস্বীকার করে গেলাম। মোটামুটি মানিয়েও ফেলেছিলাম, কিন্তু তারপর ওরা ফকিরকে দেখতে পেয়ে গেল। একজন গার্ড ওকে চিনে ফেলল। বলল, ওর নৌকোতেই শেষ দেখা গিয়েছিল আপনাকে।”
“ও মাই গড!” পিয়া বলল। “ছুঁচোমুখো একটা গার্ড?”
“হ্যাঁ। সেরকমই দেখতে। অন্যদের ও কী বলল জানি না, কিন্তু ফকিরকে তো নিয়ে জেলে পুরে দিয়েছিল আর একটু হলে। কোনও রকমে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শেষে ওদের নিরস্ত করলাম।”
“কী করে করলেন?”
খুব শুকনো গলায় কানাই বলল, “কী করে আর করব? আমার দু-একজন বন্ধুবান্ধবের নাম বললাম, আর তারপর একটু গল্পগুজব করে ওরা চলে গেল।”
পিয়া আন্দাজ করল ব্যাপারটার গুরুত্ব খানিকটা হালকা করার জন্যই এই শ্লেষের সুর কানাইয়ের গলায়। ধীর, নাগরিক স্বভাবের মানুষটার প্রতি হঠাৎ একটা কৃতজ্ঞতাবোধে ভরে উঠল ওর মন। আজকে যদি কানাই এখানে না থাকত কী হত তা হলে? খুব সম্ভবত ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের মোটরবোটে গিয়ে ওঠাই কপালে ছিল ওর।
কানাইয়ের হাতের ওপর একটা হাত রাখল পিয়া। “থ্যাঙ্ক ইউ। আপনি যা করলেন তার তুলনা নেই। এক বর্ণও বাড়িয়ে বলছি না। ফকিরও নিশ্চয়ই খুবই কৃতজ্ঞ।”
ঠাট্টা করে মাথা নোয়াল কানাই। “আপনাদের কৃতজ্ঞতা আমি মাথায় করে নিলাম।” তারপর একটু গম্ভীর হয়ে বলল, “তবে একটা কথা আমি বলব পিয়া, ফিরে যাওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু একবার সিরিয়াসলি ভেবে দেখবেন। যদি ওরা আপনাকে খুঁজে পেয়ে যায় তা হলে কিন্তু ভীষণ ঝামেলায় পড়বেন। জেলেও যেতে হতে পারে। সে ক্ষেত্রে আর আমার বা অন্য কারও খুব একটা কিছু করার থাকবে না। বর্ডার এলাকার হিসাব কেতাব কিন্তু অন্য সব জায়গার থেকে আলাদা।”
দূর জলের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল পিয়া। ওর মনে পড়ল একশো বছর আগে যখন ব্লিথ কি রক্সবার্গের মতো প্রকৃতিবিদরা এই অঞ্চল চষে বেড়িয়েছেন তখন জলচর প্রাণীতে থিকথিক করত এখানকার নদীনালা। তারপরের এই এতগুলো বছরের কথা মনে পড়ল ওর কোনও না কোনও কারণে ওই সব প্রাণীদের প্রতি আর কেউ বিশেষ নজর দেয়নি; ফলে কীভাবে ওরা আস্তে আস্তে হারিয়ে গেল সে খোঁজও রাখা হয়নি। এতদিন পরে ওর ওপরই প্রথম দায়িত্ব পড়েছে সরেজমিনে দেখে রিপোর্ট তৈরি করার। সে দায়িত্ব ও কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারবে না।
“এখন ফিরে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না কানাই,” পিয়া বলল। “আসলে, আমার কাজটা ঠিক কতটা ইম্পর্ট্যান্ট সেটা আপনাকে আমি বোঝাতে পারব না। আমি যদি আজকে ফিরে চলে যাই, আবার কবে একজন সিটোলজিস্ট এখানে আসতে পারবে কে বলতে পারে? যতদিন সম্ভব হয় আমাকে থাকতেই হবে এখানে।”
ভুরু কোঁচকাল কানাই। “আর যদি ওরা আপনাকে জেলে পুরে দেয় তা হলে কী হবে?”
কাঁধ ঝাঁকাল পিয়া। “জেলে আর কতদিন রাখবে? আবার যখন ছেড়ে দেবে, যা যা দেখেছি সেগুলো তো আমার মাথায় রয়েই যাবে, তাই না?”
.
সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়ে এল। সূর্য গনগন করছে মাথার ওপর। কাজ থামিয়ে খানিকক্ষণের জন্য কানাইয়ের পাশে তেরপলের ছায়ায় এসে বসল পিয়া। চোখের দৃষ্টি একটু যেন ক্লিষ্ট। সেটা লক্ষ করে কানাই বলল, “আপনি কি এখনও ওই ফরেস্ট গার্ডদের কথা ভাবছেন নাকি?”
কথাটা শুনে মনে হল যেন একটু চমকে উঠল পিয়া। “না না, সেসব কিছু নয়।”
“তা হলে?”
মাথা পেছনে হেলিয়ে পিয়া ওয়াটার বটল থেকে একটু জল খেল। মুখটা মুছে নিয়ে বলল, “ওই গ্রামটার কথা ভাবছি। কালকে রাত্রের কথা। কিছুতেই আমি ঘটনাটা বের করতে পারছি না মাথা থেকে–ঘুরে ফিরে ছবিগুলো চোখের সামনে ভেসে আসছে–ওই লোকগুলোর ছবি, আগুনের ছবি.. যেন অন্য কোনও যুগের একটা ঘটনা–ইতিহাস লেখা শুরু হওয়ার আগেকার কোনও সময়ের। মনে হচ্ছে কখনওই মন থেকে আমি দূর করতে পারব না ওই…”
মনে মনে ঠিক শব্দটা হাতড়াতে লাগল পিয়া। শূন্যস্থান পূরণ করার জন্যে কানাই বলল: “ওই বিভীষিকা?”
“বিভীষিকা। হ্যাঁ। জীবনে কখনও ভুলতে পারব কি না জানি না।”
“সম্ভবত না।”
“কিন্তু ফকির বা হরেন বা গ্রামের অন্য সব লোকেরা ওদের কাছে তো এটা রোজকার জীবনের অংশ, তাই না?”
“আমার মনে হয় পিয়া, এইভাবেই জীবনটাকে নিতে শিখেছে ওরা। তা ছাড়া ওরা বাঁচতে পারবে না।”
“সেই চিন্তাটাই তাড়া করে বেড়াচ্ছে আমাকে,” বলল পিয়া। তার মানে ওরাও তো এই বিভীষিকারই অংশ হয়ে গেল, ঠিক না?”
হাতের নোটবইটা ঝপ করে বন্ধ করে দিল কানাই। “ফকির কিংবা হরেনের মতো মানুষদের প্রতি অবিচার না করে যদি পুরো ব্যাপারটা দেখতে চান পিয়া, হলে কিন্তু আমি বলব বিষয়টা ঠিক এতটা সহজ নয়। মানে, আমি বলতে চাইছি সেভাবে দেখতে গেলে আমরাও কি এক হিসেবে ওই বিভীষিকার অংশ নই? আপনি বা আমি বা আমাদের মতো লোকেরা?”
নিজের ছোট ছোট কোকড়া চুলে আঙুল বোলাল পিয়া। “ঠিক বুঝলাম না।”
“ওই বাঘটা দু-দুটো মানুষ মেরেছে, পিয়া, কানাই বলল। “আর সেটা শুধু একটা মাত্র গ্রামে। এই সুন্দরবনে প্রতি সপ্তাহে লোক মারা পড়ে বাঘের হাতে। সেই বিভীষিকাটার কথা একবার ভেবে দেখেছেন কি? পৃথিবীর অন্য কোথাও যদি এই হারে মানুষ মরত তা হলে সেটাকে তো গণহত্যা বলা হত। কিন্তু এখানে এই নিয়ে সেরকম কোনও কথাই ওঠে না। এইসব মৃত্যুগুলোর কথা কোথাও লেখা হয় না, খবরের কাগজওয়ালারাও এই নিয়ে কখনও হইচই ফেলে না। কারণটা কী? না, এই মানুষগুলো এতটাই গরিব যে এরা মরল কি বাঁচল তাতে কারওর কিছু এসে যায় না। এই কথাগুলো আমরা সবাই জানি, কিন্তু জেনেশুনেও চোখ বন্ধ করে থাকি। একটা জানোয়ারের কষ্ট হলে আমাদের গায়ে লাগে, কিন্তু মানুষের কষ্টে কিছু এসে যায় না সেটা বিভীষিকা নয়?”
“কিন্তু একটা কথা আমাকে বলুন কানাই, সারা পৃথিবীতে প্রতিদিনই তো ডজন ডজন মানুষ মরছে রাস্তাঘাটে, গাড়িতে, অ্যাক্সিডেন্টে। এটা তার চেয়ে বেশি ভয়াবহ কেন বলছেন?” পালটা প্রশ্ন করল পিয়া।
“কারণ এর পেছনে আমাদেরও হাত রয়েছে পিয়া, সেইজন্যে।”
অস্বীকারের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল পিয়া। এখানে আমার হাত কীভাবে রয়েছে বুঝতে পারলাম না।”
“কারণ আপনার মতো লোকেরাই এখানে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য বার বার চাপ দিয়েছেন,” কানাই বলল। “আর তার জন্য মানুষকে কী দাম দিতে হবে তার তোয়াক্কাও করেননি। আর আমিও দায়ী তার কারণ আমার মতো মানুষেরা মানে আমার শ্রেণীর ভারতীয়রা–সেই দামের হিসেবটাকে কখনও প্রকাশ হতে দেয়নি, যাতে পশ্চিমি দেশগুলোর সুনজরে থাকতে পারে সেইজন্য। যে মানুষগুলো মরছে তাদের পাত্তা না দেওয়াটা খুব একটা কঠিন না, কারণ তারা গরিবস্য গরিব। একবার নিজেকেই জিজ্ঞেস করি দেখুন, পৃথিবীর আর কোনও জায়গায় কেউ এটা চলতে দেবে? মার্কিন দেশের কথা যদি ভাবেন, সেখানে বন্দি বাঘের সংখ্যা ভারতবর্ষে মোট যত বাঘ আছে তার থেকে বেশি। তারা যদি একবার মানুষ মারতে শুরু করে তা হলে কী হবে একবার বলুন দেখি?”
“কিন্তু কানাই, বন্দি অবস্থায় কোনও প্রজাতির সংরক্ষণ আর তাকে তার নিজের জায়গায় রেখে সংরক্ষণের মধ্যে একটা বড় তফাত আছে,” পিয়া বলল।
“তফাতটা ঠিক কী শুনি?”
“তফাতটা হল,” ধীরে ধীরে প্রতিটা শব্দের ওপর জোর দিয়ে পিয়া বলল, “প্রাণীগুলো যে এইভাবে বাঁচবে শুরু থেকে এটাই নির্দিষ্ট ছিল। আর সেটা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল প্রকৃতি–আপনি বা আমি নই। একবার ভাবুন তো, আমরা ছাড়া আর কোনও প্রজাতি জগতে রইল কি মরল তাতে কিছু যায় আসে না–এরকম একটা ভাবনার থেকে যে কাল্পনিক রেখাটা আমাদের ঠেকিয়ে রেখেছে, সেটা যদি একবার পেরিয়ে যাই তা হলে কী হবে? কতটুকু অবশিষ্ট থাকবে তা হলে? এই ব্রহ্মাণ্ডে আমরা তো যথেষ্টই একা, কানাই। আর সেখানেই কি সবকিছু থেমে থাকবে মনে করেছেন? একবার যদি আমরা স্থির করি যে অন্য সব জীবজন্তুকে মেরে সাফ করে দেওয়ার অধিকার আমাদের আছে, তারপরে তো শেষে মানুষ মারা শুরু হবে। যে মানুষগুলোর কথা আপনি বলছেন–গরিব অবহেলিত তারাই শিকার হবে তখন।”
“কথাগুলো বলেছেন ভালই পিয়া, কিন্তু আপনাকে তো আর প্রাণ দিয়ে তার দাম দিতে হচ্ছে না।”
“যদি দরকার হয় সে দাম আমি দিতে পারব না মনে করছেন?” চ্যালেঞ্জ করল পিয়া।
“মানে আপনি বলছেন আপনি মরতেও রাজি আছেন?” কানাই টিটকিরির সুরে প্রশ্ন করল। “কী যে বলেন পিয়া।”
খুব শান্ত গলায় পিয়া বলল, “আমি একবর্ণও মিথ্যে দাবি করছি না কানাই। যদি জানতাম আমার প্রাণের মূল্যে এই নদীগুলো আবার ইরাবড়ি ডলফিনদের জন্যে নিরাপদ হয়ে উঠবে, তা হলে আমার জবাব হল, হ্যাঁ। সেরকম ক্ষেত্রে মরতেও রাজি আছি আমি। কিন্তু সমস্যাটা হল আমি বা আপনি বা এরকম হাজারটা লোক মরলেও কোনওই সমাধান হবে না এ সমস্যার।”
“এসব কথা বলা তো খুবই সোজা–”
“সোজা?” শুকনো বিরক্তির সুর পিয়ার গলায়। “একটা কথা বলুন তো কানাই, যে কাজগুলো আমি করি তার কোনওটাই কি আপনার খুব সোজা মনে হয়? আমার দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন তো আমার ঘরবাড়ি নেই, টাকাপয়সা নেই, জীবনে উন্নতি করার কোনও আশা নেই। আমার বন্ধুবান্ধবরা আমার থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে, কপাল যদি ভাল থাকে খুব বেশি হলে বছরে একবার তাদের সঙ্গে দেখা হয় আমার। আর সেটাও তো কিছুই না। তার চেয়েও বড় কথা হল, আমি ভাল করেই জানি যে কাজটা আমি করছি শেষ পর্যন্ত তার সবটাই মোটামুটি ব্যর্থ হবে।”
মুখ তুলে তাকাল পিয়া। কানাই দেখল ওর চোখে টলটল করছে জল।
“সোজা কাজ এটা আদৌ নয় কানাই। কথাটা আপনাকে ফিরিয়ে নিতে হবে।”
একটা কড়া জবাব ঠোঁটের ডগায় চলে এসেছিল, কোনওরকমে সেটা গিলে ফেলল কানাই। তার বদলে পিয়ার একটা হাত নিজের দু’হাতের মধ্যে ধরে বলল, “সরি পিয়া। এভাবে বলা উচিত হয়নি আমার। কথাটা ফিরিয়ে নিলাম।”
হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল পিয়া। বলল, “যাই, কাজ করি গিয়ে।”
নিজের জায়গার দিকে এগিয়ে গেল পিয়া। পেছন থেকে ডেকে কানাই বলল, “আপনি কিন্তু খুব সাহসী মেয়ে, সেটা জানেন কি?”
অস্বস্তিতে কাঁধ ঝাঁকাল পিয়া। “আমি আমার নিজের কাজটা করছি শুধু।”
.
মিস্টার স্লোয়েন
দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকেল, ভাটাও শেষ হতে চলেছে, এমন সময় দূরে দেখা গেল গর্জনতলা। আস্তে আস্তে মেঘা এগিয়ে চলল দহটার দিকে। দূরবিন হাতে ডেকের ওপর দাঁড়িয়েছিল পিয়া। ডলফিনের দঙ্গলটা চোখে পড়তেই খুশিতে ওর মনটা নেচে উঠল। জোয়ার-ভাটার সময় মেনে ঠিক এসে হাজির হয়েছে ওরা। দহ থেকে মেঘা তখনও কিলোমিটার খানেক দূরে। কিন্তু ডলফিনগুলোর নিরাপত্তার কথা ভেবে সেখানেই নোঙর ফেলতে ইশারা করল পিয়া।
এর মধ্যে কখন কানাই এসে দাঁড়িয়েছে পাশে। পিয়া জিজ্ঞেস করল, “কাছ থেকে দেখতে চান নাকি ডলফিনগুলোকে?”
“নিশ্চয়ই,” জবাব দিল কানাই। “যে জানোয়ারদের কাছে মনপ্রাণ সঁপে দিয়েছেন আপনি তাদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে তো আমি উদগ্রীব হয়ে আছি।”
“চলে আসুন তা হলে। আমরা ফকিরের নৌকোয় করে যাব।”
বোটের পেছন দিকটায় গিয়ে ওরা দেখল দাঁড় হাতে নিয়ে অপেক্ষা করছে ফকির। ডিঙিতে উঠে পিয়া গিয়ে গলুইয়ের ওপর নিজের জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে পড়ল, আর কানাই বসল নৌকোর মাঝামাঝি একটা জায়গায়।
খানিকক্ষণ দাঁড় টেনে সোজা দহটার মধ্যে পৌঁছে গেল ফকির। আর খানিক পরেই দুটো ডলফিন দল ছেড়ে এগিয়ে এল নৌকোর দিকে। তারপর পাক খেতে লাগল ডিঙিটাকে ঘিরে। ডলফিনদুটোকে চিনতে পেরে খুশি হয়ে উঠল পিয়া। সেই মা আর তার ছানাটা। পিয়ার মনে হল–আগেও ওর এরকম মনে হয়েছে ওর্কায়েলাদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে ওকেও যেন চিনতে পেরেছে ডলফিনগুলো। কারণ নৌকোর পাশে পাশে বারবার ভেসে উঠছিল ওরা। বড়টা তো মনে হল সোজাসুজি তাকাল ওর চোখের দিকে।
কানাই এদিকে খানিকটা অবাক হয়ে ভুরু কুঁচকে লক্ষ করছিল প্রাণীগুলোকে। শেষে খানিকটা অবিশ্বাসের সুরে প্রশ্ন করল, “এগুলোই আপনার সেই ডলফিন তো? ঠিক জানেন আপনি?”
“অবশ্যই। এক্কেবারে ঠিক জানি।”
“কিন্তু একবার দেখুন ওদের দিকে,” কানাইয়ের গলায় পরিষ্কার অভিযোগের সুর। “খালি তো ভাসছে আর ডুবছে, আর ঘোঁতঘোঁত করছে।”
“এ ছাড়াও আরও অনেক কিছু ওরা করে কানাই,” বলল পিয়া। “কিন্তু সেসবের বেশিরভাগটাই করে জলের তলায়।”
“আমি তো ভেবেছিলাম আপনি আমাকে আমার মবি ডিক দেখাতে নিয়ে যাচ্ছেন,” কানাই বলল। “কিন্তু এ তো দেখছি জলের শুয়োর কতগুলো।”
হেসে ফেলল পিয়া। “আপনি কাদের কথা বলছেন জানেন কানাই? এরা কিন্তু খুনে তিমির খুড়তুতো ভাই।”
“শুয়োরদেরও অনেক সময় বড় বড় সব আত্মীয়স্বজন থাকে জানেন তো?” কানাই বলল।
“কানাই, ওর্কায়েলাদের সঙ্গে শুয়োরের চেহারার একেবারেই কোনও মিল নেই।”
“তা বটে, এগুলোর পিঠের ওপর কী একটা যেন আছে।”
“ওটাকে বলে ফিন–পাখনা।”
“আর এগুলো শুয়োরের মতো অতটা সুস্বাদুও হবে না বোধহয়।”
“কানাই, স্টপ ইট।”
কানাই হাসল। “আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না, এই হাস্যকর শুয়োর প্যাটার্নের কতগুলো জন্তু দেখার জন্য এতদূর থেকে এত কষ্ট করে এসেছি আমরা। একটা জন্তুর জন্য যখন আপনি জেলে যেতেও রাজি আছেন, তখন আরেকটু সেক্স অ্যাপিল-ওয়ালা আর কিছু খুঁজে পেলেন না? এদের তো কোনও রকমেরই কোনও অ্যাপিলই নেই দেখছি।”
“ওর্কায়েলাদের অ্যাপিল কিছু কম নেই কানাই,” বলল পিয়া। “আপনাকে শুধু একটু ধৈর্য ধরতে হবে সেটা আবিষ্কার করার জন্য।”
রসিকতার সুরে কথা বললেও, কানাইয়ের বিস্ময়টা কিন্তু নির্ভেজাল। ওর মনে যে ডলফিনের ছবি ছিল সে হল সিনেমা কি অ্যাকুয়ারিয়ামে দেখা চকচকে ধূসর রঙের একটা জন্তু। হ্যাঁ, তার প্রতি একটা আকর্ষণ তৈরি হলেও হতে পারে। কিন্তু এই নৌকোর চারপাশে ভেসে বেড়ানো বোতামচোখো হাঁসফঁসে জানোয়ারগুলোর মধ্যে ইন্টারেস্টিং তো কিছুই নেই। ভুরু কোঁচকাল কানাই। “আপনি কি গোড়া থেকেই ঠিক করে রেখেছিলেন যে এই জন্তুগুলোর পেছন পেছন সারা পৃথিবী চষে বেড়াবেন?”
“না। সেটা বলতে পারেন একটা অ্যাক্সিডেন্ট,” পিয়া বলল। “প্রথম যখন আমি ওর্কায়েলা ডলফিন দেখি, এদের সম্পর্কে তখন কিছুই জানতাম না আমি। সে প্রায় বছর তিনেক আগের কথা।”
দক্ষিণ চিন সাগরে স্তন্যপায়ী জলজন্তুদের ওপর সার্ভের কাজ করছিল একটা দল, তাদের সঙ্গে ইন্টার্ন হিসেবে গিয়েছিল পিয়া। সার্ভের শেষে ওদের জাহাজ গিয়ে থামল কম্বোডিয়ার পোর্ট সিহানুকে। সেখান থেকে দলের কয়েকজন চলে গেল নম পেন, সেখানে এক আন্তর্জাতিক বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংস্থায় তাদের কিছু বন্ধু কাজ করে সেই বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে। সেই তখনই মধ্য কম্বোডিয়ার এক ছোট্ট গ্রামে আটকে পড়া একটা নদীচর ডলফিনের কথা ওরা জানতে পারল।
“ভাবলাম যাই, একবার দেখে আসি গিয়ে।”
জায়গাটা দেখা গেল নম পেন থেকে ঘণ্টা খানেকের দূরত্বে, মেকং নদী থেকে অনেকটা ভেতরে। একটা ভাড়া করা মোটর সাইকেলের পেছনে চড়ে সেখানে গিয়ে পৌঁছল পিয়া। গ্রামটা দেখতে খানিকটা তালি দেওয়া কাপড়ের মতো–এখানে ওখানে কিছু কুঁড়েঘর, ধানক্ষেত, জলসেচের নালা, আর কয়েকটা অগভীর জলা। এরকমই একটা জলার মধ্যে–মাপে সেটা খুব বেশি হলে একটা সুইমিং পুলের মতো হবে–আটকে পড়েছিল ডলফিনটা। বর্ষার সময় বানের জলে যখন থইথই করছিল চারদিক সেই সময়েই এসে ঢুকেছিল, কিন্তু কোনও কারণে দলের বাকিদের সঙ্গে ফিরে যেতে পারেনি আর। বর্ষা কেটে যেতে এদিকে চাষের নালা-টালাও সব গেছে শুকিয়ে, ফলে বেরোনোর সব পথও বন্ধ হয়ে গেছে।
সেই প্রথম একটা ওর্কায়েলা ব্রেভিরোষ্ট্রিস চোখে দেখল পিয়া। লম্বায় প্রায় মিটার খানেক, চওড়ায় তার অর্ধেক, ছাই ছাই রঙের শরীর, আর পিঠের ওপর একটা পাখনা। সাধারণত ডলফিনদের মুখের সামনের দিকটা যেমন হাঁসের ঠোঁটের মতো দেখতে হয়, সেরকম কোনও কিছুর কোনও বালাই নেই। গোল মাথা আর বড় বড় চোখের প্রাণীটাকে দেখে অদ্ভুত লাগল পিয়ার, মনে হল খানিকটা গোরু জাতীয় জাবর কাটা কোনও জন্তুর মতো দেখতে। ডলফিনটার নাম দিয়েছিল ও মিস্টার স্লোয়েন, ওর স্কুলের এক টিচারের নাম। ভদ্রলোকের চেহারার সঙ্গে হালকা একটা সাদৃশ্য ছিল জন্তুটার।
খুবই ফ্যাসাদে পড়েছিল এই মিস্টার স্লোয়েন। ডোবাটার জল দ্রুত শুকিয়ে আসছে, সব মাছও গেছে ফুরিয়ে। মোটর সাইকেল ড্রাইভারের সঙ্গে পাশের কামপংটায় গিয়ে কিছু মাছ কিনে নিয়ে এল পিয়া বাজার থেকে। বাকি সারাটা দিন ধরে ওই ডোবার পারে বসে নিজের হাতে সবগুলো মাছ খাওয়াল ডলফিনটাকে। পরের দিন আবার গেল সেখানে, একটা কুলার ভর্তি মাছ সঙ্গে নিয়ে। আশ্চর্য ব্যাপার, গ্রামের অনেক চাষিবাসি বাচ্চাকাচ্চা সব ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল জলাটার ধারে, কিন্তু পিয়া যেই গেল, তাদের কাউকে পাত্তা না দিয়ে সোজা ওর দিকে চলে এল প্রাণীটা।
“বাজি রেখে বলতে পারি আমাকে চিনতে পেরেছিল ও।”
এদিকে তো নম পেনে যে কয়জন পশুপ্রেমী ছিল তারা খুবই চিন্তায় পড়ে গেছে। মেকং-এর ওর্কায়েলাদের সংখ্যা খুবই দ্রুত কমে আসছে, আর কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো হাতের বাইরে চলে যাবে পরিস্থিতি। কম্বোডিয়ার দুর্দিনে যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে মেকং ওর্কায়েলাদেরও। ১৯৭০-এর দশকে মার্কিনি কার্পেট বম্বিং-এর শিকার হয়েছে ওরা। আর তারপর খুমের রুজদের সময়ে ওর্কায়েলারাও হাজারে হাজারে মরেছে ওদের হাতে। পেট্রোলিয়ামের জোগান ক্রমশ কমে আসায় বিকল্প জ্বালানি হিসেবে ডলফিনের তেল ব্যবহার করতে শুরু করেছিল খুমেররা। কম্বোডিয়ার সবচেয়ে বড় মিঠে জলের হ্রদ টোনলে স্যাপের অগুন্তি ডলফিন একটা সময় প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল এভাবে। রাইফেল আর বোমা ছুঁড়ে ডলফিন মারা হত তখন, তারপর তাদের ঝুলিয়ে রাখা হত রোদের মধ্যে। সূর্যের তাপে তাদের চর্বি গলে গলে পড়ত নীচে রাখা বালতিতে। তারপর মোটর সাইকেল আর নৌকো চালানোর কাজে লাগত সেই চর্বি। ২৮৬
“মানে, আপনি বলতে চাইছেন ডলফিনের চর্বি গলিয়ে তাই দিয়ে ডিজেলের কাজ চালানো হত?” কানাই জিজ্ঞেস করল।
“ঠিক তাই।” গত কয়েক বছর ধরে নানা কারণে আরও বেশি করে বিপন্ন হয়ে পড়েছে কম্বোডিয়ার এই ওর্কায়েলারা। মেকং নদীর উজানে পাথর ফাটিয়ে খাত চওড়া করার একটা পরিকল্পনা হচ্ছে, যাতে করে সোজা চিন দেশ পর্যন্ত নৌ চলাচল সহজ হয়ে যাবে। সেই মতো কাজ যদি এগোতে থাকে, তা হলে এই ডলফিনদের কিছু কিছু স্বাভাবিক বসতি নষ্ট হয়ে যাবে। অর্থাৎ মিস্টার স্লোয়েনের এই দুর্দশা কোনও একটি প্রাণীর সমস্যা নয়–এ হল গোটা একটা প্রজাতির বিপর্যয়ের সংকেত।
ডলফিনটাকে নদীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করার সময়ে পিয়াকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল প্রাণীটার দেখাশোনা করার। ছ’দিন ধরে প্রত্যেক সকালে কুলার ভর্তি মাছ নিয়ে ও চলে যেত জলাটার ধারে। সাত দিনের দিন গিয়ে দেখল মিস্টার স্লোয়েনের কোনও চিহ্ন নেই সেখানে। শুনল আগের দিন রাত্রে নাকি মারা গেছে ডলফিনটা। কিন্তু সেই খবরের সমর্থনে কোনও প্রমাণ ও খুঁজে পেল না। জলার মধ্যে থেকে প্রাণীটার শেষ চিহ্ন পর্যন্ত কীভাবে লোপাট হয়ে গেল তারও কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না। যেটা চোখে পড়ল তা হল জলার ধারের কাদায় ভারী কোনও গাড়ির–খুব সম্ভবত একটা ট্রাকের–টায়ারের দাগ। জলের একেবারে কাছাকাছি গিয়ে শেষ হয়েছে দাগটা। কী ঘটেছে সেটা বুঝতে ওদের একটুও অসুবিধা হয়নি–বেআইনি কোনও বন্যপ্রাণী পাচার চক্রের শিকার হয়েছে মিস্টার স্লোয়েন। পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় নতুন নতুন অ্যাকুয়ারিয়াম ভোলা হচ্ছে, সে জন্য নদীর ডলফিনের চাহিদা দিনে দিনে বাড়ছে। সে বাজারে মিস্টার স্লোয়েনের দাম অনেক। এই একটা ইরাবড়ি ডলফিন এক লাখ মার্কিন ডলারে পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে এরকমও শোনা গেছে।
“এক লাখ ডলার?” কানাইয়ের গলায় অবিশ্বাস। এই জন্তুগুলোর জন্যে?”
“হ্যাঁ।”
জানোয়ার নিয়ে আদিখ্যেতার স্বভাব পিয়ার কোনওকালে ছিল না, কিন্তু মিস্টার স্লোয়েন একটা দর্শনীয় সামগ্রী হিসেবে কোনও অ্যাকুয়ারিয়ামে বিক্রি হয়ে যাবে–কথাটা ভাবতেই ওর মাথার ভেতরে কেমন করতে লাগল। তারপর বেশ কয়েকদিন ধরে ওর স্বপ্নে ঘুরে ঘুরে আসতে লাগল একটা ছবি–একদল শিকারি জলাটার এক ধারে কোণঠাসা করে ফেলছে মিস্টার স্লোয়েনকে, তাদের হাতে মাছ ধরার জাল।
ব্যাপারটা মন থেকে মুছে ফেলার জন্য পিয়া ঠিক করল আবার আমেরিকায় ফিরে যাবে। সেখানে লা জোলার স্ক্রিপ্স ইন্সটিটিউটে ভর্তি হবে পি এইচ ডি করার জন্য। কিন্তু তার মধ্যেই একটা অদৃষ্টপূর্ব ঘটনা ঘটে গেল : নম পেনের এক বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংস্থা মেকং ওর্কায়েলাদের ওপর সার্ভে করার জন্য একটা কন্ট্রাক্ট দিতে চাইল ওকে। সব দিক থেকেই ভাল ছিল অফারটা। যে টাকা ওরা দিতে চাইছিল সেটা বছর দুয়েক চালিয়ে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট, তা ছাড়া ও ভেবে দেখল এই সার্ভেটা করলে ওর পি এইচ ডি-র কাজটাও খানিকটা এগিয়ে যাবে। কাজটা নিয়েই নিল পিয়া। মেকং-এর উজানে ক্রেতি নামের এক আধঘুমন্ত শহরে গিয়ে আস্তানা গাড়ল। তারপর তিন বছরের মধ্যে হাতে গোনা কয়েকজন ওর্কায়েলা বিশেষজ্ঞদের একজন হয়ে উঠল ও। সারা পৃথিবীর যেখানে যেখানে ওর্কায়েলা ডলফিনদের দেখা পাওয়া যায় সেইসব জায়গায় গিয়ে সার্ভের কাজ করল পিয়া–বার্মা, উত্তর অস্ট্রেলিয়া, ফিলিপাইন্স, থাইল্যান্ড–সব জায়গায়। কেবল একটা জায়গা ছাড়া। প্রথম যেখানে এই ডলফিনরা প্রাণিতত্ত্ববিদদের রেকর্ড বইয়ে জায়গা পেয়েছিল, সেই ইন্ডিয়াতে এসে কাজ করা ওর হয়ে ওঠেনি।
কাহিনির একেবারে শেষের দিকে এসে পিয়ার খেয়াল হল নৌকোয় উঠে অবধি ফকিরের সঙ্গে একটাও কথা বলেনি। সেটা মনে পড়ে একটু খারাপ লাগল ওর।
কানাইকে ডেকে বলল, “আচ্ছা, একটা ব্যাপার আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। দেখুন, ফকির তো এই এলাকাটাকে, এই গর্জনতলা দ্বীপটাকে মনে হয় খুব ভালভাবে চেনে। ডলফিনদের সম্পর্কেও অনেক কিছু জানে–ওরা কোথা থেকে আসে, কোথায় যায়… আমার জানতে ইচ্ছে করে প্রথম কীভাবে ও এই জায়গাটায় এল, এইসব কথা ও কীভাবে জানল। আপনি একটু জিজ্ঞেস করবেন ওকে?”
“নিশ্চয়ই।” ফকিরের দিকে ফিরে পিয়ার প্রশ্নটা ব্যাখ্যা করল কানাই। তারপর ফকির তার জবাব শুরু করতেই পিয়ার দিকে ঘুরে বসল ও। “ও যা বলছে সেটা শোনাচ্ছি আপনাকে।”
“প্রথম কবে এই জায়গার কথা জানলাম সেটা মনেই পড়ে না আমার। যখন খুব ছোট্ট ছিলাম, এইসব দ্বীপ নদী কিছু চোখেই দেখিনি, তখন থেকেই মায়ের কাছে গর্জনতলার গল্প শুনেছি। মা আমাকে গান গেয়ে গেয়ে শোনাত, এই দ্বীপটার গল্প বলত। মা বলেছিল যার মনে কোনও পাপ নেই এই দ্বীপে তার কোনও ভয় নেই।
“আর এই বড় শুশদের কথা জিজ্ঞেস করছেন? ওদের কথাও আমি জানতাম, এখানে আসার অনেক আগেই। শুশদের সব গল্পও মা বলত আমাকে। বলত ওরা হল বনবিবির দূত, এখানকার নদীনালার সব খবর ওরাই পৌঁছে দেয় বনবিবিকে। মা বলেছিল ওরা ভাটার সময় এখানে আসে, যাতে ভাল করে সব দেখে-টেখে গিয়ে বনবিবিকে বলতে পারে। আর জোয়ার এলেই বনের ধারে ধারে ছড়িয়ে গিয়ে বনবিবির চোখ-কান হয়ে যায়। এই গোপন খবরটা দাদু বলেছিল মাকে। বলেছিল শুশুকদের পেছন পেছন চলতে যদি শিখতে পার তা হলে মাছ পেতে কখনও কোনও অসুবিধা হবে না।
“এই ভাটির দেশে আসার অনেক আগেই আমি এসব গল্প শুনেছি। ছোটবেলা থেকেই আমার মনে তাই এই জায়গাটা দেখার খুব ইচ্ছে ছিল। তারপর আমরা যখন মরিচঝাঁপিতে থাকতে এলাম, আমি প্রায়ই মাকে বলতাম, কবে যাব মা? কবে আমরা গর্জনতলা যাব? কিন্তু সময়ই হত না–এত কাজ ছিল মা-র তখন। মারা যাওয়ার সপ্তাহ কয়েক আগে মা প্রথম আমাকে নিয়ে এসেছিল এখানে। সেজন্যেই হয়তো তারপর থেকে মা-র কথা মনে পড়লেই অমনি গর্জনতলার কথাও মনে পড়ে যেত আমার। পরে কতবার আমি এসেছি এখানে। আস্তে আস্তে এই শুশরাও আমার বন্ধুর মতো হয়ে গেল। ওরা যেখানে যেত আমিও ওদের পেছন পেছন গেছি কতবার।
“‘সেদিন আপনি যখন ওই ফরেস্টের লোকেদের সঙ্গে লঞ্চে করে এসে আমার নৌকো থামালেন, তখনও আমি আমার ছেলেকে নিয়ে এখানেই আসছিলাম। তার আগের দিন রাত্রে আমার মা স্বপ্নে এসেছিল। বলল, আমি তোর ছেলেকে দেখতে চাই। ওকে কখনও গর্জনতলায় নিয়ে আসিস না কেন? তোর তো আর কিছুদিনের মধ্যেই আমার কাছে চলে আসার সময় হয়ে যাবে, তারপর ওকে আমি আবার কবে দেখতে পাব কে জানে? যত তাড়াতাড়ি পারিস ওকে নিয়ে আয়।’
“আমি আমার বউকে এসব কথা বলতে পারিনি। বিশ্বাসই করবে না আমাকে। মাঝখান থেকে খেপে যাবে। তাই পরের দিন টুটুলকে স্কুলে না নিয়ে গিয়ে নৌকোয় তুলে সোজা এখানে আসার জন্য বেরিয়ে পড়েছিলাম। পথে এক জায়গায় থেমেছিলাম কিছু মাছ ধরার জন্যে, সেই সময়েই আপনি এলেন লঞ্চে করে।”
“তারপর কী হল? তোমার মা কি ওকে দেখতে পেয়েছিলেন মনে হয়?” জিজ্ঞেস করল পিয়া।
“হ্যাঁ। আগের দিন যখন এখানে রাতের বেলায় নৌকোয় ঘুমোচ্ছিলাম, আবার স্বপ্নে মাকে দেখতে পেলাম আমি। খুব খুশি হয়েছে। বলল, খুব ভাল লাগল তোর ছেলেকে দেখে। যা, এবার ওকে গিয়ে বাড়িতে রেখে আয়। তারপর আমরা আবার একসাথে হব।”
এতক্ষণ পর্যন্ত মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনে যাচ্ছিল পিয়া। কানাইয়ের অস্তিত্বের কথা যেন ভুলেই গিয়েছিল প্রায়, কেমন একটা ঘোরের মধ্যে মনে হচ্ছিল যেন সরাসরি ফকিরের সঙ্গেই কথা বলছিল ও। কিন্তু হঠাৎ ঘোরটা ভেঙে গেল এবার, পিয়া যেন চমকে জেগে উঠল ঘুমের থেকে।
“এটা ও কী বলছে কানাই?” ও প্রশ্ন করল। “জিজ্ঞেস করুন না, এটা কী বলতে চাইছে ও?”
“ও বলছে এটা একটা স্বপ্ন দেখেছিল শুধু।”
পিয়ার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে ফকিরকে কী যেন একটা বলল কানাই। আর তারপরেই হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে পিয়া শুনল ফকির একটা গান গাইতে শুরু করেছে, অথবা গানও ঠিক বলা যায় না সেটাকে, মনে হল যেন খুব দ্রুত লয়ে একটা কিছু মন্ত্র বলছে।
“ও কী বলছে ওটা?” কানাইকে জিজ্ঞেস করল পিয়া। “ইংরেজি করে বলে দিতে পারবেন আপনি?”
“সরি পিয়া,” জবাব দিল কানাই। “এ আমার ক্ষমতার বাইরে। ফকির বনবিবির উপাখ্যান থেকে গাইছে–খুব জটিল ছন্দটা। এটা আমার দ্বারা হবে না।”
.
ক্রেতি
বেলা বাড়ার সাথে সাথে দিক বদলাল নদীর স্রোত। জল যেই বাড়তে আরম্ভ করল, শুশুকগুলোও সরে যেতে লাগল দহটা থেকে। আস্তে আস্তে শেষ ডলফিনটাও যখন চলে গেল, মেঘার দিকে ডিঙির মুখ ফিরিয়ে দাঁড় টানতে শুরু করল ফকির।
ইতিমধ্যে হরেন আর তার নাতি মিলে লঞ্চের পেছন দিকটায় কয়েকটা তেরপল খাঁটিয়ে স্নানের জন্য একটা ঘেরা জায়গা তৈরি করে ফেলেছে। সারাটা দিন রোদের মধ্যে কাটানোর পর ভাল করে স্নান করার এরকম সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইল না পিয়া। তোয়ালে সাবান নিয়ে চটপট ঢুকে পড়ল ঘেরাটোপের ভেতর। দুটো বালতি রাখা রয়েছে সেখানে, তার মধ্যে একটা ভর্তি, আর অন্যটার হাতলের সঙ্গে একটা লম্বা দড়ি বাঁধা রয়েছে জল তোলার জন্য। নদীতে ছুঁড়ে দিল সেটাকে পিয়া। জলটা তুলে পুরো বালতি উপুড় করে ঢালল মাথায়। শিরশিরে ঠান্ডায় গা-টা যেন জুড়িয়ে গেল একেবারে। অন্য বালতিটায় ভর্তি করে পরিষ্কার জল রাখা ছিল। একটা এনামেলের মগে করে তার থেকে একটু একটু করে নিয়ে গায়ের সাবানটা ধুয়ে নিল। স্নান হয়ে যাওয়ার পরেও অর্ধেকটা মতো জল রয়ে গেল বালতিতে।
কেবিনে ফেরার পথে কানাইয়ের সঙ্গে দেখা হল। কাঁধে একটা তোয়ালে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল ডেকের একধারে।
“অনেকটা পরিষ্কার জল রেখে এসেছি আপনার জন্যে।”
“যাই, সেটার সদ্ব্যবহার করে আসি তা হলে।”
খানিক দূর থেকে ঝপাৎ ঝপাৎ করে আরেকটা কারও গায়ে জল ঢালার আওয়াজ কানে এল। নিশ্চয়ই ফকির, স্নান করছে নিজের ডিঙিতে।
একটু বাদে ধোয়া জামাকাপড় পরে ডেকের ওপর এসে দাঁড়াল পিয়া। ভরা জোয়ারে থই থই করছে নদী, নোঙর করা বোটের গায়ে ধাক্কা খেয়ে স্রোতের ঘূর্ণি নানা রকম নকশা তৈরি করছে। দূরে কয়েকটা দ্বীপ ছোট হয়ে সরু চড়ার মতো দেখা যাচ্ছে। খানিক আগে যে জায়গাটা ছিল জঙ্গল, সেখানে এখন গাছের কয়েকটা ডাল শুধু চোখে পড়ছে, নলখাগড়ার মতো দুলছে স্রোতের টানে।
একটা চেয়ার টেনে নিয়ে রেলিং-এর ধারে বসতে যাচ্ছে পিয়া, এমন সময় কানাই এসে পাশে দাঁড়াল। দু’হাতে ধোঁয়া ওঠা দুটো চায়ের কাপ। পিয়াকে একটা দিয়ে বলল, “হরেন পাঠাল নীচে থেকে।”
কানাইও একটা চেয়ার নিয়ে বসল পিয়ার পাশে। চারপাশের দ্বীপ-জঙ্গল আস্তে আস্তে কেমন তলিয়ে যাচ্ছে, দেখতে লাগল মগ্ন হয়ে। পিয়ার মনে হল এই বোধহয় কানাই কোনও ঠাট্টার কথা বলে উঠবে, কিংবা ট্যারাবাঁকা মন্তব্য করবে কিছু একটা; কিন্তু সেসব কিছুই করল না কানাই, চুপচাপ বসে রইল শান্ত হয়ে। তবে তার মধ্যেও একটা উষ্ণ আন্তরিকতা বেশ অনুভব করা যাচ্ছিল। নীরবতা ভেঙে শেষে পিয়াই শুরু করল কথা বলতে।
“মনে হয় আমি যেন সারা জীবন ধরে বসে বসে এই জোয়ার ভাটার খেলা দেখে যেতে পারি।”
“দ্যাটস ইন্টারেস্টিং,” বলল কানাই। “আমি এক সময় একটি মেয়েকে জানতাম যে প্রায় এই একই রকমের একটা কথা বলত–সমুদ্র সম্পর্কে।”
“কোনও গার্লফ্রেন্ড?”
“হ্যাঁ।”
“অনেক গার্লফ্রেন্ড আছে বুঝি আপনার?”
মাথা ঝাঁকাল কানাই। তারপর হঠাৎ যেন আলোচনাটা ঘোরানোর জন্যই জিজ্ঞেস করল, “আর আপনার? সিটোলজিস্টদেরও কি ব্যক্তিগত জীবন-টিবন বলে কিছু থাকে?”
“জিজ্ঞেস করলেন যখন বলি,” পিয়া বলল, “খুব কম সিটোলজিস্টেরই সেটা থাকে। বিশেষ করে মহিলাদের তো থাকেই না প্রায়। যে ধরনের রুটিনের মধ্যে দিয়ে আমাদের চলতে হয় তাতে ব্যক্তিগত সম্পর্ক-টম্পর্ক গড়ে ওঠা খুবই কঠিন।”
“কেন?”
“এত ঘোরাঘুরি করতে হয় আমাদের”…বলল পিয়া। “কোনও একটা জায়গায় এক টানা বেশি দিন থাকাই হয়ে ওঠে না। ফলে, ব্যাপারটা খুব একটা সহজ নয়।”
ভুরুদুটো একটু তুলে কানাই জিজ্ঞেস করল, “এটা নিশ্চয়ই আপনি দাবি করবেন না যে আপনার কখনও কারও সঙ্গে কোনও সম্পর্ক তৈরি হয়নি–এমনকী কলেজে-টলেজেও নয়?”
“হ্যাঁ, সে কখনও কিছু হয়নি তা নয়,” পিয়া স্বীকার করল, “কিন্তু সে সম্পর্কগুলি শেষ পর্যন্ত কোথাও গিয়ে পৌঁছয়নি।”
“কখনও না?”
“শুধু একবার,” পিয়া বলল। “এই একবারই মাত্র আমার মনে হয়েছিল সম্পর্কটা সত্যি সত্যি কোথাও একটা যাচ্ছে।”
“তারপর?”
হেসে ফেলল পিয়া। তারপর আর কী? একদিন যাচ্ছেতাই ভাবে শেষ হয়ে গেল ব্যাপারটা। সেটা ঘটেছিল ক্রেতিতে।”
“ক্রেতি? সেটা আবার কোথায়?”
“পূর্ব কম্বোডিয়া,” বলল পিয়া। “নম পেন থেকে কয়েকশো কিলোমিটার দূরে। সেখানে এক সময় থাকতাম আমি।”
মেকং নদীর ভেতর ঢুকে আসা খাড়াই একটা অন্তরীপ মতো জায়গার ওপর ক্রেতি শহরটা তৈরি হয়েছে। শহর থেকে কয়েক কিলোমিটার উত্তরে নদীর মধ্যে একটা দহ আছে, গরমকালে জল কমে এলে গোটা ছয়েক ওর্কায়েলার একটা দল সেই দহটার মধ্যে থাকে। এখান থেকেই ওর রিসার্চের কাজ শুরু করেছিল পিয়া। শহরটা সুবিধাজনক জায়গাতেও বটে আর এমনিতে ছিমছাম সুন্দর, পিয়া তাই ঠিক করেছিল পরবর্তী দু-তিন বছর এখানে থেকেই রিসার্চের কাজ করবে। একটা কাঠের বাড়ির ওপরের তলাটা ভাড়া নিল ও। আরও একটা সুবিধা ছিল ক্রেতি শহরে। সরকারি মৎস্য বিভাগের একটা দফতর ছিল ওখানে। গবেষণার কাজে মাঝেমধ্যেই ওদের সাহায্য নিতে হত পিয়াকে।
সেখানে এক অল্প বয়স্ক সরকারি অফিসার ছিল সেই মৎস্যবিভাগের স্থানীয় প্রতিনিধি। দিব্যি ইংরেজি-টিংরেজি বলতে পারত। ছেলেটির নাম ছিল রথ, বাড়ি নম পেনে। ক্রেতিতে ওরও কোনও বন্ধুবান্ধব ছিল না, ফলে একা একা একটু মনমরা হয়ে থাকত। বিশেষ করে সন্ধেবেলাগুলো কাটানোই ওর কাছে ছিল এক সমস্যা। ক্রেতি ছোট্ট জায়গা, কয়েকটা পাড়া নিয়ে একটা গোটা শহর, ফলে মাঝে মধ্যেই পিয়ার দেখা হয়ে যেত রথের সঙ্গে। দেখা গেল নদীর পাড়ে যে কাফেটাতে সন্ধেবেলা পিয়া নুডল আর ওভালটিন খেতে যায়, প্রায়দিনই রথও যায় সেখানে ডিনার করতে। রোজ একই টেবিলে গিয়ে বসতে শুরু করল ওরা দু’জন, রোজকার টুকিটাকি খোশগল্প আস্তে আস্তে এক সময় সত্যিকারের কথোপকথনে মোড় নিল।
একদিন কথায় কথায় জানা গেল ছেলেবেলায় বেশ কিছুদিন রথকে পল পট জমানার এক ডেথ ক্যাম্পে কাটাতে হয়েছিল। খমের রুজ নম পেনের দখল নেওয়ার পর ওর মা-বাবাকে পাঠানো হয়েছিল সেখানে। যদিও এটা সেটা কথার মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে বিষয়টা একবার মাত্র উল্লেখ করেছিল রথ, কিন্তু পিয়া তাতে এমন নাড়া খেয়ে গেল যে হুড়মুড় করে নিজের ছেলেবেলার অনেক কথা ওকে বলে ফেলল। তার পরের কয়েকটা সপ্তাহে পিয়া দেখল এমনভাবে ও রথের সঙ্গে গল্প করছে যে ভাবে আগে আর কোনও পুরুষের সঙ্গে কখনও কথা বলেনি। রথকে ও নিজের মা-বাবার কথা বলল, তাদের বিয়ের কথা বলল, মায়ের ডিপ্রেশনের কথা, হাসপাতালে তার শেষ দিনগুলোর কথা–সব বলল।
ও যা যা বলেছিল তার কতটা বুঝতে পেরেছিল রথ? সত্যি বলতে কী, সেটা জানে না পিয়া। রথ তার নিজের জীবনের একটা বড় তথ্য পিয়াকে বলে দিয়েছে, সেটা কি একটা ভ্রান্ত ধারণা মাত্র ছিল? হয়তো নিজের সেই অভিজ্ঞতার কথা খুব সাধারণভাবেই, উল্লেখ করেছিল ও। যে সময়টাতে রথ বড় হয়েছে এই রকম ঘটনা তো তখন বিরল কিছু ব্যাপার নয় কম্বোডিয়ায়। কে জানে? সত্যিটা কোনও দিনও আর জানতে পারবে না পিয়া।
একদিন পিয়া লক্ষ করল সমস্ত সময়ই ও কেবল রথের কথাই ভাবছে, এমনকী যখন ডলফিনগুলো তাদের ওই দহটার মধ্যে কী করছে তাতে ওর মন দেওয়া উচিত, তখনও। পিয়া বুঝতে পারছিল যে ও প্রেমে পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু তাতে চিন্তিত হয়নি একটুও। তার অন্যতম প্রধান কারণ রথের স্বভাব–পিয়ার মতো ও-ও একটু চাপা ধরনের, একটু অমিশুক প্রকৃতির। ওর দ্বিধাগ্রস্ত হাবভাবে স্বস্তি পেত পিয়া, মনে হত ও নিজে যেমন পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশার বিষয়ে অনভিজ্ঞ, রথেরও হয়তো সেরকম নারীসঙ্গ বিষয়ে কোনও অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও যথেষ্ট সতর্ক ছিল পিয়া। ঘনিষ্ঠতা খাবার-দাবার আর স্মৃতির আদানপ্রদানের পরের স্তরে গড়াতে প্রায় মাস চারেক লেগে গিয়েছিল। আর তার পরে মনের যে একটা হালকা ভাব আসে সে কারণেই হয়তো নিজের স্বাভাবিক সব সতর্কতা সহজে দূরে সরিয়ে দিতে পেরেছিল ও। মনে হয়েছিল এই তো, পাওয়া গেছে এবার। মহিলা ফিল্ড বায়োলজিস্টদের মধ্যে যে সৌভাগ্য বিরল, সেই সৌভাগ্যের অধিকারিণী হতে চলেছে ও; ঠিক জায়গাতে এসে খুঁজে পেয়েছে নিজের মনের মানুষকে।
সেবার গ্রীষ্মের শেষে ছয় সপ্তাহের জন্যে হংকং যেতে হয়েছিল পিয়াকে একটা কনফারেন্সে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে, আর তা ছাড়া একটা সার্ভে টিমের সঙ্গে কাজ করে কিছু পয়সা রোজগারের জন্যে। রওনা যখন হল, মনে হয়েছিল ঠিকঠাকই চলছে সব কিছু। পোচেনতং এয়ারপোর্টে ওকে প্লেনে তুলে দিয়ে গিয়েছিল রথ, তারপর প্রথম কয়েক সপ্তাহ ই-মেলের আদানপ্রদানও হত প্রতিদিন। তারপরেই আস্তে আস্তে কমতে থাকল মেলের জবাব আসা। শেষে একটা সময় কোনও জবাবই আর আসত না রথের কাছ থেকে। রথের অফিসে ফোন করেনি পিয়া, কারণ যতটা সম্ভব খরচ বাঁচানোর চেষ্টা করছিল ও। আর তা ছাড়া, ওর মনে হয়েছিল এই কয়েকটা মাত্র সপ্তাহে আর কীই বা হতে পারে?
ফেরার সময় বোট থেকে ক্রেতিতে নামার সঙ্গে সঙ্গেই পিয়া বুঝতে পেরেছিল একটা গোলমাল কিছু হয়েছে। হেঁটে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরতে ফিরতে সারাটা পথ যেন লোকজনের চাপা গলার কথা শুনতে পাচ্ছিল ও। ওর বাড়িওয়ালিই প্রথম দিল খবরটা, কুৎসিত একটা আনন্দের আভাস ফুটে উঠেছিল মহিলার গলায় রথ বিয়ে করেছে, ট্রান্সফার নিয়ে চলে গেছে নম পেনে।
পুরো বিষয়টা গোড়া থেকে ভাবতে গিয়ে প্রথমে পিয়ার মনে হল হয়তো বাড়ির চাপে বিয়েটা করে ফেলতে বাধ্য হয়েছে রথ—সেরকম কিছু একটা ঘটে থাকতেই পারে, সেটা বোঝাটা কঠিন নয় পিয়ার পক্ষে। আর ব্যাপারটার তিক্ততাও একটু হ্রাস পায় তাতে। প্রত্যাখ্যানটা অতটা সরাসরি এসে মনে ঘা দেয় না, একটু কম নিষ্ঠুর লাগে। কিন্তু সে সান্ত্বনাটাও রইল না যখন ও জানতে পারল নিজের অফিসেরই একটি মেয়েকে বিয়ে করেছে রথ–একজন অ্যাকাউন্টান্টকে। পিয়া হংকং রওনা হওয়ার পরপরই মনে হল মেয়েটির কাছে যাতায়াত শুরু করেছিল রথ, আর মাত্র ছয় সপ্তাহ সময় লেগেছিল ওর মন স্থির করতে।
এইসব কিছু সত্ত্বেও মনে মনে রথকে ক্ষমা করতে পারত পিয়া। হয়তো ওর অনুপস্থিতিতে রথের মনে হয়ে থাকতে পারে এরকম একজন বিদেশি মেয়েকে বিয়ে করলে ভবিষ্যতে নানা রকম সমস্যা হতে পারে, তার ওপর যে বিদেশি একটানা বেশিদিন এক জায়গায় থাকেই না। সেই রকম কিছু ভেবে যদি রথ এই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে তা হলে কি ওকে দোষ দেওয়া যায়?
এই সব ভেবে মনে মনে কিছু দিন একটু শান্তি পাওয়ার চেষ্টা করেছিল পিয়া। কিন্তু সে ভুল ভেঙে গেল যেদিন রথের জায়গায় নতুন যে লোকটি এসেছে তার সঙ্গে আলাপ হল ওর। লোকটি বিবাহিত, বছর তিরিশেক বয়স, মোটামুটি ইংরেজি বলে। আলাপ হওয়ার খানিকক্ষণের মধ্যেই সে পিয়াকে নিয়ে গেল নদীপাড়ের সেই কাফেতে, যেখানে এক সময় নিয়মিত যেত রথ আর পিয়া। দূরে মেকঙের অন্য পাড়ে তখন সূর্য ডুবছে। লোকটি পিয়ার চোখের দিকে তাকিয়ে ওর মা-র সম্পর্কে নানা সহানুভূতিসূচক প্রশ্ন করতে শুরু করল। পিয়া বুঝতে পারল রথ সবকিছু বলে দিয়েছে এই লোকটিকে, বুঝতে পারল এই শহরের প্রতিটি পুরুষ এখন জানে ওর জীবনের একান্ত সব কথা; আর ওর সামনে বসা জঘন্য ঘিনঘিনে চরিত্রের এই লোকটি সেই তথ্য ব্যবহার করে আনাড়ির মতো ওকে ভুলিয়ে দে ফেলার চেষ্টা করছে।
সেখানেই ইতি। পরের সপ্তাহেই জিনিসপত্র প্যাক করে নিয়ে পিয়া চলে গেল মেকং নদীর উজানের দিকে আরও একশো কিলোমিটার দূরে, স্টাং ত্রেং শহরে। রথের ব্যবহার থেকে যে কষ্ট ও পেয়েছিল সে কষ্টের যন্ত্রণা নয়, সারা শহরের কাছে নিজের জীবনটা উদোম হয়ে যাওয়ার গ্লানিই ওকে শেষে তাড়িয়ে ছাড়ল ক্রেতি থেকে।
“কিন্তু ধাক্কা খাওয়ার আরও বাকি ছিল আমার,” পিয়া বলল।
“কী সে ধাক্কাটা?”
“সেটাও ঘটল আমি আমেরিকায় ফিরে যাওয়ার পর। কয়েকজন পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল আমার। এরা সকলেই মহিলা, সকলেই ফিল্ড বায়োলজিস্ট। ওরা সবাই খুব হাসল আমার গল্পটা শুনে। ওদের প্রত্যেকের জীবনে কোথাও না কোথাও হুবহু এই একই রকম ঘটনা ঘটেছে। যে যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে আমাকে যেতে হয়েছে সে যেন আমার নিজের জীবনের ঘটনা নয়, যেন আগে থেকে লিখে রাখা কোনও কাহিনি, যে কাহিনির চরিত্রযাপন আমাদের সকলের নিয়তি। এটাই বাস্তব, ওরা বলল আমাকে। বলল : এই রকমই হবে তোমার জীবন, জেনে রেখো। সব সময়ই দেখবে কোনও না কোনও একটা ছোট শহরে গিয়ে তোমাকে থাকতে হচ্ছে, সেখানে কথা বলার কেউ নেই, শুধু এই একটা মাত্র লোক যে কিছুটা ইংরেজি জানে। তাকে তুমি কিছু বলা মাত্রই সারা শহরে চাউর হয়ে যাবে তা। কাজেই এখন থেকে আর মুখটি কোথাও খুলো না, আর একা একা থাকতে অভ্যেস করো।”
কাঁধ ঝাঁকাল পিয়া। “তো সেটাই আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি তার পর থেকে।”
“কী?”
“একা নিজের মনে থাকার অভ্যাস করা।” চুপ করে গেল কানাই। পিয়ার গল্পটার কথা ভাবতে লাগল মনে মনে। মনে হল এ পর্যন্ত পিয়ার মধ্যেকার মানুষটাকে দেখতেই পায়নি ও। পিয়ার সংযত আত্মস্থ ভাব আর কম কথা বলার অভ্যাস কানাইকে–এমনকী নিজের কাছেও– স্বীকার করতে দেয়নি পিয়ার সত্যিকারের অসাধারণত্ব; মনে আর কল্পনায় ও যে শুধু কানাইয়ের সমকক্ষ তাই নয়, ভেতরের শক্তিতে আর হৃদয়ে ও অনেক অনেক বড় কানাইয়ের চেয়ে। ২৯৪
বোটের রেলিঙের ওপর পা তুলে পেছনের দিকে একটু হেলে বসেছিল কানাই এতক্ষণ। চেয়ারটাকে সোজা করে নিয়ে একটু এগিয়ে বসল এবার। পিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, “এভাবে আর আপনাকে থাকতে হবে না পিয়া। নিজের মনে একা একা কাটাতে হবে না আর।”
“কোনও সমাধান পেলেন নাকি?”
“পেয়েছি।” কিন্তু আর কিছু বলার আগেই নীচের ডেক থেকে হরেনের গলার আওয়াজ ভেসে এল। খেতে ডাকছে।
.
চিহ্ন
আজকেও তাড়াতাড়ি শুতে চলে গেল পিয়া। আগের রাতে ঘুম ভাল হয়নি, তাই কানাইও একটু আগেভাগেই শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুম বিশেষ হল না। বেশ জোরে হাওয়া বইছিল বাইরে, আর ভটভটির দুলুনির সাথে সাথে যেন ছেলেবেলার একটা দুঃস্বপ্ন বার বার ফিরে আসছিল কানাইয়ের তন্দ্রায় একটানা একই পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছে বার বার, সেই স্বপ্ন। তফাতটা শুধু পরীক্ষকদের চেহারায়। ইস্কুলের মাস্টারমশাইদের মুখগুলোর বদলে সেখানে ভেসে আসছিল কুসুম আর পিয়া, নীলিমা আর ময়না, হরেন আর নির্মলের ছবি। শেষ রাতের দিকে হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসল কানাই, ঘামে ভিজে গেছে সারা গা : ঠিক কোন ভাষায় স্বপ্ন দেখছিল মনে পড়ল না, কিন্তু একটা শব্দই খালি ঘুরছিল ওর মাথার মধ্যে–‘পরীক্ষা’।
আধো ঘুমে কানাই বোঝার চেষ্টা করছিল কেন অপ্রচলিত পুরনো ইংরেজিতে ও অনুবাদ করতে চাইছিল শব্দটাকে : ‘ট্রায়াল বাই অর্ডিয়াল’–যন্ত্রণাদায়ক কঠোর বিচার। একেবারে ভোর পর্যন্ত ফিরে ফিরে আসতে থাকল স্বপ্নটা। তারপর অবশেষে ঘুম হল খানিকটা–গাঢ় গভীর ঘুম। বাঙ্ক থেকে যখন নামল কানাই, সকালের কুয়াশা ততক্ষণে কেটে গেছে। আর খানিকক্ষণ পরেই অন্য দিকে ঘুরে যাবে নদীর স্রোত।
কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে কানাই দেখল একটুও হাওয়া বইছে না কোনওদিকে, নদীর জল একেবারে স্থির, পালিশ করা ধাতুর পাতের মতো বিছিয়ে রয়েছে। ভরা জোয়ারে থইথই করছে নদী, জলের স্রোত পূর্ণ ভারসাম্যের বিন্দুতে এসে পৌঁছেছে, মনে হচ্ছে নদীটা যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক জায়গায়। ডেক থেকে গর্জনতলা দ্বীপটাকে মনে হচ্ছিল বিশাল একটা রুপোর ঢালের ধার বরাবর খোদাই করে বসানো দামি পাথরের সাজের মতো। দৃশ্যটা একই সঙ্গে যার পর নাই পার্থিব এবং অত্যন্ত রকম একান্ত; বিস্তারে বিশাল, আবার এই নিস্তরঙ্গ শান্তির মুহূর্তে কেমন বেমানান কোমলতাময়।
কার যেন পায়ের শব্দ শোনা গেল ডেকের ওপর। ফিরে তাকিয়ে কানাই দেখল পিয়া আসছে। হাতে ক্লিপবোর্ড আর ডেটাশিট। কেজো গলায় কানাইকে জিজ্ঞেস করল, “একটা কাজ করে দেবেন আমাকে? শুধু আজকে সকালটার জন্যে?”
“নিশ্চয়ই করে দেব। বলুন কী করতে হবে।”
“ডলফিনদের ওপর নজরদারির কাজ একটু করে দিতে হবে আমাকে,” পিয়া বলল। আসলে জোয়ার-ভাটার সময়টা পালটে যাওয়ায় একটু সমস্যায় পড়েছে পিয়া। শুরুতে ওর প্ল্যান ছিল জোয়ার এলে ডলফিনগুলো যখন দহটা ছেড়ে চলে যায়, তখন ওদের পেছন পেছন যাবে। কিন্তু এখন জোয়ারের সময়টা পালটে গেছে। জল বাড়তে শুরু করছে খুব ভোরের দিকে আর একেবারে সন্ধেবেলায়। তার মানে কোনওবারই শুশুকগুলোর দহ ছেড়ে যাওয়ার সময়টায় দিনের আলো পাওয়া যাবে না। এমনিতেই ওদের আসা-যাওয়া বোঝা যথেষ্ট কঠিন, আলো কম থাকলে তো সেটা একেবারেই অসম্ভব। পিয়া তাই ঠিক করেছে আপাতত ডলফিনগুলোর ফিরে আসার পথের একটা হিসেব রাখবে ও। ওর প্ল্যান হল দহটায় ঢোকার দুটো মুখে নজরদারির ব্যবস্থা করবে–একটা উজানের দিকে, আরেকটা ভাটির দিকে। উজানের দিকে নজর রাখবে ও নিজে, মেঘার ডেক থেকে। নদী সেখানে অনেকটা চওড়া, দূরবিন ছাড়া ওদিকটায় লক্ষ রাখা কঠিন। আর অন্যদিকটায় ফকির নজর রাখতে পারে তার ডিঙি থেকে। কানাইও যদি তার সঙ্গে থাকতে পারে তা হলে খুবই ভাল হয়–দূরবিনের অভাব দু’জোড়া চোখ খানিকটা পূরণ করতে পারবে।
“তার মানে আপনাকে কয়েকটা ঘণ্টা ফকিরের সঙ্গে ওর নৌকোয় কাটাতে হবে,” পিয়া বলল। “কিন্তু তাতে নিশ্চয়ই আপনার কোনও সমস্যা নেই?”
ফকিরের সঙ্গে ওর কোনও রকমের প্রতিযোগিতা আছে–এরকম একটা চিন্তা পিয়ার মনে এসেছে বলে আঁতে একটু ঘা লাগল কানাইয়ের। তাড়াতাড়ি বলল, “না না। ওর সঙ্গে কথা বলার একটা সুযোগ পাওয়া গেলে আমি তো খুশিই হব।”
“গুড। তাই ঠিক রইল তা হলে। আপনি কিছু খেয়ে-টেয়ে নিন, তারপরেই বেরিয়ে পড়া যাবে। ঘণ্টাখানেক পরে আমি ডেকে নেব আপনাকে।”
.
পিয়া যতক্ষণে ডাকতে এল তার মধ্যে ব্রেকফাস্ট সেরে বেরোনোর জন্যে একেবারে তৈরি হয়ে গেছে কানাই। সারাটা দিন রোদে রোদে কাটাতে হবে বলে হালকা রঙের ট্রাউজার্স পরেছে একটা, গায়ে সাদা জামা, আর পায়ে চপ্পল। একটা টুপি আর সানগ্লাসও সঙ্গে নিয়ে নেবে ঠিক করেছে। প্রস্তুতি দেখে সন্তুষ্ট হল পিয়া। দু’বোতল জল হাতে দিয়ে বলল, “এগুলোও রেখে দিন সঙ্গে। প্রচণ্ড গরম হবে কিন্তু ওখানে।”
একসঙ্গে বোটের পেছন দিকটায় গিয়ে ওরা দেখল ফকিরও বেরোনোর জন্যে তৈরি হয়ে বসে আছে, দাঁড়দুটো রাখা আছে নৌকোর ওপর, আড়াআড়ি ভাবে। কানাই ডিঙিতে গিয়ে ওঠার পরে পিয়া ফকিরকে দেখিয়ে দিল ঠিক কোন জায়গাটায় নৌকোটা নিয়ে গিয়ে রাখতে হবে। মেঘা এখন যেখানে আছে সেখান থেকে জায়গাটা দু’ কিলোমিটার মতো দূরে, ভাটির দিকে। গর্জনতলা দ্বীপ্টা ওইখানটাতে বাইরের দিকে একটু বেঁকে গেছে, খানিকটা ঢুকে এসেছে নদীর ভেতর; ফলে খাতটা সরু হয়ে গেছে একটু। “মাত্র এক কিলোমিটারের মতো চওড়া হবে নদীটা ওই জায়গায়,”পিয়া বলল। “আমার মনে হয় ফকির যদি ঠিক মাঝনদীতে নোঙর করে, তা হলে ওদিক দিয়ে যে ডলফিনগুলো আসবে, আপনারা দুজনে মিলে সেগুলোর সবকটার ওপরেই নজর রাখতে পারবেন।
তারপর উজানের দিকে একটা জায়গা দেখিয়ে বলল, “আর আমি থাকব ওইখানটায়।” সেখানে বিশাল একটা মোহনায় গিয়ে মিশেছে নদীটা। “দেখতেই পাচ্ছেন ওখানে নদী অনেকটা চওড়া, কিন্তু লঞ্চে থাকব বলে খানিকটা উঁচু থেকে দেখতে পাব আমি। আর দূরবিনও থাকবে সঙ্গে, ফলে ওইদিকটা আমার পক্ষে সামলে নেওয়া কঠিন হবে না। আমরা মোটামুটি কিলোমিটার চারেক দূরে দূরে থাকব। আমি আপনাদের দেখতে পাব, কিন্তু আপনারা আমাকে দেখতে পাবেন বলে মনে হয় না।”
বোট থেকে কাছি খুলে নিল ফকির। পিয়া হাত নাড়ল ওদের দিকে। মুখের সামনে দুটো হাত জড়ো করে চেঁচিয়ে বলল, “যদি মনে হয় আর পারছেন না কানাই, ফকিরকে বলবেন, ও এসে বোটে দিয়ে যাবে আপনাকে।”
কানাইও হাত নাড়ল, “কিছু অসুবিধা হবে না। আমাকে নিয়ে কিছু ভাবতে হবে না আপনাকে।”
ডিঙি খানিক দূর এগোতে এগোতেই লঞ্চের চিমনি থেকে দমকে দমকে কালো ধোঁয়া বেরোতে শুরু করল। আস্তে আস্তে সরতে শুরু করল মেঘা, ইঞ্জিনের ধাক্কায় ঢেউ উঠল জলে। পরের কয়েক মিনিট ধরে সেই ঢেউয়ে ঝাঁকুনি খেতে খেতে এগোতে লাগল ফকির আর কানাই। জল আবার শান্ত হল লঞ্চটা একেবারে চোখের আড়ালে চলে যাওয়ার পর।
গোটা জায়গাটা জনমানবশূন্য হয়ে যাওয়ার পর এবার কানাইয়ের আর ফকিরের মধ্যে দূরত্ব যেন শতগুণে কমে গেল। তবুও, নৌকোটা যদি দু’কিলোমিটার লম্বা হত, ততটাই দূরে থাকত ওরা একে অপরের থেকে। ডিঙির একেবারে সামনের দিকে বসেছিল কানাই, আর ফকির ছিল পেছনে, ছইয়ের আড়ালে। মাঝখানে ছইয়ের বেড়াটা থাকার জন্য কেউ কাউকে দেখতেও পাচ্ছিল না। জলের ওপরে প্রথম ঘণ্টা কয়েক কোনও কথাও বিশেষ হয়নি দু’জনের মধ্যে। বার দুয়েক কানাই কথা বলার চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু প্রতিবারই দায়সারা একটা দুটো হু হা ছাড়া বিশেষ কোনও জবাব পায়নি।
দুপুর নাগাদ, জল যখন নামতে শুরু করেছে, হঠাৎ খুব উত্তেজিত হয়ে লাফিয়ে উঠল ফকির। ভাটির দিকে ইশারা করে বলল, “ওই যে–ওইখানে।”
চোখের ওপর হাত আড়াল করে কানাই দেখল সরু খাঁজকাটা তেকোনা একটা পাখনা বাঁক খেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে জল কেটে।
“ছইটা ধরে উঠে দাঁড়ালে আরও ভাল করে দেখতে পাবেন।”
“ঠিক আছে।” প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে নৌকোর মাঝামাঝি জায়গাটায় গিয়ে পৌঁছল কানাই, উঠে দাঁড়াল কোনওরকমে, ছইয়ের বাতায় হেলান দিয়ে টাল সামলে নিল।
“আরেকটা। ওই যে, ওইখানটায়।”
ফকিরের আঙুল বরাবর তাকিয়ে জল কেটে এগোনো আরও একটা পাখনা দেখতে পেল কানাই। সামান্য পরেই আরও দুটো ডলফিন দেখা গেল–ফকিরই দেখতে পেয়েছে সবগুলো।
হঠাৎ এই হুড়োহুড়িতে ফকিরের নীরবতার বেড়ায় ছোট্ট একটু ফাঁক তৈরি হয়েছে মনে হল, কানাই তাই আরেকবার চেষ্টা করল ওকে কথাবার্তায় টেনে আনতে। “আচ্ছা ফকির, একটা কথা বলো তো আমাকে,” ছইয়ের ওপর দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল কানাই, “সারের কথা তোমার একটুও মনে আছে?”
চট করে কানাইয়ের দিকে একবার তাকিয়ে ফের অন্যদিকে চোখ সরিয়ে নিল ফকির। বলল, “না একটা সময় উনি খুব আসতেন আমাদের এখানে, কিন্তু তখন তো আমি খুব ছোট। মা মারা যাওয়ার পরে ওনাকে আর বিশেষ দেখিনি আমি। ওনার কথা কিছুই প্রায় মনে নেই আমার।”
“আর তোমার মা? তার কথা মনে আছে তোমার?”
“মা-কে কী করে ভুলব বলুন? মা-র মুখ তো সব জায়গায়।”
এমন সহজ সাধারণ ভাবে কথাটা ও বলল যে একটু হকচকিয়ে গেল কানাই।.”কী বলছ ফকির? কোথায় মা-র মুখ দেখো তুমি?”
একটু হেসে ফকির সব দিকে ইশারা করে দেখাতে লাগল। কম্পাসের সবগুলো দিক ছাড়াও নিজের মাথার দিকে আর পায়ের দিকেও দেখাল : “এদিকে দেখি, এদিকে দেখি, এদিকে দেখি, এদিকে দেখি। সব জায়গায় দেখি।”
এত সরল বাক্যগঠন যে প্রায় শিশুর কথা বলার মতো শুনতে লাগল সেটা। কানাইয়ের মনে হল অবশেষে ও বুঝতে পেরেছে সব কিছু সত্ত্বেও ময়নার কেন এমন গভীর টান তার স্বামীর প্রতি। ফকিরের স্বভাবের মধ্যে কিছু একটা এখনও খুব কঁচা অবস্থায় রয়ে গেছে, আর সেটাই ময়নাকে টানে; নরম মাটির দলা সামনে পেলে কুমোরের হাত যেমন নিশপিশ করে, ফকিরের জন্য সেভাবেই নিশপিশ করে ময়নার মন।
“আচ্ছা ফকির, তোর শহরে যেতে ইচ্ছে করে না কখনও?”
কথাটা বলেই কানাইয়ের খেয়াল হল, নিজের অজান্তেই তুমি থেকে তুই-এ নেমে এসেছে ও, যেন সত্যি সত্যিই ফকির আসলে বাচ্চা একটা ছেলে। ফকির কিন্তু সেসব লক্ষ করেছে বলে মনে হল না। “এখানেই আমার ভাল,” জবাব দিল ও। “শহরে গিয়ে আমি কী করব?” তারপরে, কথাবার্তা শেষ করার জন্যেই যেন দাঁড় তুলে নিল হাতে। “এবার লঞ্চে ফিরে যাওয়ার সময় হয়েছে।”
জলে দাঁড় ডোবাতেই দুলে উঠল নৌকো। তাড়াতাড়ি গলুইয়ের ওপর নিজের জায়গাটায় গিয়ে বসল কানাই। বসার পর তাকিয়ে দেখল ফকির জায়গা পালটেছে। এখন ও ডিঙির ঠিক মাঝামাঝি জায়গায়; এমনভাবে বসেছে যাতে দাঁড় টানার সময় মুখটা কানাইয়ের দিকে ফেরানো থাকে। ঝলসানো গরমের ভাপ উঠছে নদী থেকে, মনে হচ্ছে যেন মরীচিকা নাচছে জলের ওপর। গরমে আর জল থেকে ওঠা ভাপে আস্তে আস্তে কেমন ঘোর লেগে গেল কানাইয়ের, যেন স্বপ্নের মধ্যে ফকিরের একটা ছবি ভেসে এল ওর চোখের সামনে ফকির যেন সিয়াটেল যাচ্ছে পিয়ার সঙ্গে। দেখতে পেল ওরা দু’জনে প্লেনে গিয়ে উঠছে, পিয়ার পরনে জিনস আর ফকির পরে আছে লুঙ্গি আর একটা ধুন্ধুড়ে টি-শার্ট দেখতে পেল একটা সিটের ওপর কুঁকড়ে বসে আছে ফকির জীবনে সেরকম সিট ও চোখে দেখেনি; হাঁ করে আইলের এপাশ থেকে ওপাশ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। তারপর পশ্চিমের হিমঠান্ডা কোনও শহরে ফকিরকে কল্পনা করল কানাই, কাজের খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস্তায় রাস্তায়, ঘুরতে ঘুরতে পথ হারিয়ে ফেলেছে, কিন্তু কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারছে না।
অপ্রীতিকর ছবিটা চোখের সামনে থেকে তাড়ানোর জন্যে মাথা ঝাঁকাল কানাই।
ওর মনে হল যে পথে ওরা এসেছিল তার তুলনায় গর্জনতলা দ্বীপের অনেক কাছ দিয়ে যাচ্ছে এখন। কিন্তু জল একেবারে নীচে নেমে গেছে বলে বোঝা মুশকিল যে ইচ্ছে করেই পথ পালটেছে ফকির, না ভাটার সময় নদী সরু হয়ে গেছে বলে চোখের ভুলে এরকম মনে হচ্ছে। দ্বীপের পাশ দিয়ে যেতে যেতে হাতের তালুতে রোদ আড়াল করে বাঁদিকে তাকাল ফকির। পাড়টা ঢালু হয়ে সেখানে নেমে এসেছে জলে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ টানটান হয়ে গেল ওর পেশিগুলো, সোজা হয়ে একটু উঠে বসল। ডান হাতে যন্ত্রের মতো লুঙ্গির আলগা দিকটা তুলে কেঁচা মেরে নিল, ল্যাঙোটের মতো হয়ে গেল অত বড় কাপড়টা। আধা-হামাগুড়ি অবস্থায় নৌকোর ধারে হাতের ভর দিয়ে শরীরটা সামনে ঝুঁকিয়ে দিল–খেলার মাঠে দৌড় শুরু করার সময় লোকে যে ভাবে দাঁড়ায়, অনেকটা সেই ভঙ্গিতে। অল্প টলমল করে উঠল ডিঙি। হাত তুলে পাড়ের দিকে ইশারা করল ফকির : “দেখুন, ওই জায়গাটায় দেখুন।”
“কী ব্যাপার?” জিজ্ঞেস করল কানাই। “কী দেখছিস তুই ওখানে?”
হাত তুলে দেখাল ফকির : “দেখুন না।”
চোখ কুঁচকে ওর আঙুল বরাবর তাকাল কানাই, কিন্তু দেখার মতো কিছু চোখে পড়ল না। জিজ্ঞেস করল, “কী দেখব?”
“দাগ, চিহ্ন–কালকে যেমন দেখেছিলাম সেইরকম। সোজা চলে গেছে খোঁচগুলো, দেখতে পাচ্ছেন না? ওই ঝোঁপটার কাছ থেকে জল পর্যন্ত এসে আবার ফিরে গেছে।”
ভাল করে ফের একবার দেখল কানাই। মনে হল কয়েকটা জায়গায় মাটি যেন বসে বসে গেছে একটু। কিন্তু কাদা থেকে উঠে থাকা গর্জনগাছের ছুঁচোলো শ্বাসমূলে একেবারে ভর্তি জায়গাটা। মাটির তলার শেকড় থেকে বের হয়ে আসা এই মূলগুলো দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ চালায় এ গাছ। খাড়া হয়ে থাকা বর্শার মতো সেই শুলোর ভিড়ে একটা দাগ থেকে আরেকটা দাগের তফাত করা একেবারে অসম্ভব।
মাটি দেবে যাওয়া যে দাগ এখানে ফকিরের চোখে পড়েছে, গতকালের দেখা স্পষ্ট ছোপগুলোর সঙ্গে তার কোনও মিলই নেই। কানাইয়ের মনে হল নির্দিষ্ট কোনও আকৃতিহীন এই দাগগুলো থেকে পরিষ্কার ভাবে কিছুই বলা যায় না; এগুলো এমনকী কঁকড়ার গর্ত বা জল নামার সময় স্রোতের টানে তৈরি খাতও হতে পারে।
“দেখছেন কেমন একটা লাইন ধরে গেছে খোঁচগুলো?” ফকির বলল। “একেবারে জলের ধার পর্যন্ত চলে গেছে। তার মানে জল নেমে যাওয়ার পরে হয়েছে–এগুলো হয়তো যখন আমরা এদিকে আসছিলাম, সেই সময়। জানোয়ারটা নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছে আমাদের। আরও ভাল করে দেখার জন্যে তাই নেমে এসেছিল।”
ওরা মোহনা পেরিয়ে এগোচ্ছে, সেটা ভাল করে দেখার জন্যে একটা বাঘ জলের ধার পর্যন্ত নেমে আসছে–এই পুরো ভাবনাটাই এত কষ্টকল্পিত, যে হাসি পেয়ে গেল কানাইয়ের।
“আমাদের কেন দেখতে চাইবে?” ফকিরকে জিজ্ঞেস করল ও।
“আপনার গন্ধ পেয়েছে হয়তো। নতুন লোকেদের চোখে চোখে রাখতে ভালবাসে এ জানোয়ার।”
ফকিরের হাবভাবের মধ্যে এমন কিছু একটা ছিল যাতে কানাইয়ের দৃঢ় ধারণা হল ও একটা খেলা খেলছে কানাইয়ের সঙ্গে, হয়তো নিজের অজান্তেই। কথাটা ভেবে বেশ মজা লাগল ওর। পরিস্থিতির পরিবর্তনই হয়তো ফকিরকে প্রলুব্ধ করেছে চারপাশের এই ভয়াল রূপকে আরও বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলতে। ব্যাপারটা বুঝতে বিশেষ অসুবিধা হল না কানাইয়ের। ওকেও অনেকবার ফকিরের মতো এভাবে নিরুপায় কোনও বিদেশির সামনে অচেনা জগতের জানালা খুলে দেওয়ার কাজ করতে হয়েছে। মনে পড়ল, সেসব সময়ে ওরও অনেকবার কেমন লোভ হয়েছে সূক্ষ্মভাবে চারপাশের জগৎকে একটু তির্যক করে দেখানোর, অচেনা জায়গাকে আরও রহস্যময় করে তোলার। মনের কোনায় কোনও বিদ্বেষই যে সব সময় মানুষকে দিয়ে এরকম করায় তা নয়, এটা আসলে বাইরের লোকের সামনে ভেতরের লোকের অপরিহার্যতাকে চোখে আঙুল দিয়ে বোঝানোর একটা উপায়–প্রতিটি নতুন বিপদের সম্ভাবনায় প্রমাণ হয়ে যায় কতটা গুরুত্বপূর্ণ তার উপস্থিতি, প্রতিটি নতুন সমস্যা তার দাম বাড়িয়ে দেয় বিদেশির কাছে। গাইড আর অনুবাদকদের সামনে এ প্রলোভনের হাতছানি সব সময়ই থাকে–সে হাতছানি উপেক্ষা করলে নিজের অপরিহার্যতা বজায় রাখা কঠিন, আবার তার কাছে আত্মসমর্পণ করলে কথার দাম বলেও আর কিছু থাকে না, পুরো কাজটাই হয়ে যায় মূল্যহীন। আর এই দ্বিধার ব্যাপারটা কানাইয়ের কাছে অপরিচিত নয় বলেই এটাও ও জানে যে অনুবাদককে কখনও কখনও যাচাই করে নিতে হয়।
পাড়ের কাদার দিকে দেখিয়ে অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কানাই। একটু হেসে বলল, “ধুর, এ তো এমনি গর্ত। দেখা যাচ্ছে কাঁকড়ারা মাটি খুঁড়ছে ওগুলোর মধ্যে। এ দাগগুলো বড় শেয়ালের তুই কী করে বুঝলি?”
ওর দিকে ফিরে হাসল ফকির। ঝকঝক করে উঠল সাদা দাঁতগুলো। “কী করে বুঝলাম দেখবেন?”
একটু ঝুঁকে কানাইয়ের একটা হাত টেনে নিয়ে নিজের ঘাড়ের ওপর রাখল ও। আচমকা এই স্পর্শের ঘনিষ্ঠতায় একটা যেন ঝটকা লাগল কানাইয়ের হাতে। একটানে হাতটা সরিয়ে নিতে নিতে কানাই টের পেল ফকিরের ভেজা চামড়ায় কাটা কাটা হয়ে ফুটে উঠেছে। রোমকূপগুলো।
আবার ওর দিকে তাকিয়ে হাসল ফকির। বলল, “দেখলেন তো কী করে বুঝলাম? ভয় দিয়েই বুঝতে পারি আমি।” তারপর উবু হয়ে একটু উঠে বসে সপ্রশ্ন চোখে তাকাল কানাইয়ের দিকে। জিজ্ঞেস করল, “আর আপনি? আপনি ভয় টের পাচ্ছেন না?”
কথাগুলো কানাইয়ের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া তৈরি করল স্বতস্ফূর্ততায় তার সঙ্গে ফকিরের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠার খুব একটা তফাত নেই। চেতনা থেকে হঠাৎ মুছে গেল এই বাদাবন, জল আর নৌকোর পারিপার্শ্বিক; এ মুহূর্তে ও কোথায় বসে আছে সে কথা ভুলে গেল কানাই। ওর মন যেন ফিরে যেতে চাইল নিজের চেনা কাজের বৃত্তে যে কাজের অভ্যাসে জড়িয়ে আছে দীর্ঘ দিনের অনুশীলন আর তিল তিল করে গড়ে ওঠা দক্ষতা। এই মুহূর্তে ওর ভাবনায় ভাষা ছাড়া আর কিছুরই কোনও অস্তিত্ব নেই, ফকিরের প্রশ্নের শুদ্ধ ধ্বনি-কাঠামোটুকুই এখন ওর চেতনার সবটা জুড়ে রয়েছে। মনকে যতটা সম্ভব একাগ্র করে প্রশ্নটা বিচার করল কানাই। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উত্তরটা মনে এসে গেল : নেতিবাচক উত্তর। ফকিরের গায়ে যেরকম ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে, কানাইয়ের আদৌ সেরকম ভয় লাগছে না। এমনিতে যে ও অসাধারণ সাহসী সেরকম বলা যায় না–তা ও একেবারেই নয়। কিন্তু এটাও কানাই জানে যে সাধারণত যেরকম বলা হয়ে থাকে ভয় জিনিসটা আদৌ সেরকম জন্মগত কোনও প্রবৃত্তি নয়। মানুষ ভয় পেতে শেখে; পূর্বজ্ঞান, অভিজ্ঞতা আর আজন্ম শিক্ষার থেকেই আস্তে আস্তে ভয় জমে ওঠে মনের মধ্যে। ভয়ের অনুভূতি কারও সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার থেকে কঠিন কাজ আর কিছু হতে পারে না। আর এই মুহূর্তে যে ভীতির সঞ্চার ফকিরের মনের মধ্যে হয়েছে, সে ভীতি এতটুকুও অনুভব করতে পারছে না কানাই।
“জিজ্ঞেস করলি তাই বলছি,” কানাই জবাব দিল, “সত্যি কথাটা হল, না। আমার ভয় লাগছে না। তুই যেরকম ভয় পাচ্ছিস সেরকম তো পাচ্ছিই না।”
পুকুরের জলের ওপর যেমন বৃত্তাকার ঢেউ ছড়িয়ে যায়, সেরকম একটা হঠাৎ জেগে-ওঠা আগ্রহের ভাব ফকিরের সারা মুখে ছড়িয়ে গেল। সামনে একটু ঝুঁকে এসে জিজ্ঞেস করল, “ভয় যদি না পান, তা হলে আরও একটু কাছ থেকে গিয়ে দেখতেও আপনার নিশ্চয়ই কোনও অসুবিধা নেই? কী বলেন?”
একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ফকির, চোখের পলক পড়ছে না। কানাইও নিজেকে চোখ নামিয়ে নিতে দেবে না কিছুতেই। বাজি দ্বিগুণ করে দিয়েছে ফকির, ওকে এখন ঠিক করতে হবে কী করবে পিছিয়ে যাবে, না যাচাই করে নেবে ফকিরের কথাটা।
মনের মধ্যে একটু অনিচ্ছার ভাব যদিও ছিল, তা সত্ত্বেও কানাই বলল, “ঠিক আছে। যাওয়া যাক তা হলে।”
মাথা নাড়ল ফকির। একটা দড়ে জল টেনে ঘুরিয়ে নিল ডিঙি। নৌকোর মুখ পাড়ের দিকে ফিরতে বাইতে শুরু করল তারপর। জলের দিকে একবার তাকাল কানাই : পালিশ করা পাথরের মেঝের মতো শান্ত নদী, তার ওপরে খোদাই করা স্রোতের নকশাগুলো মনে হচ্ছে যেন স্থির হয়ে আছে একেবারে, মার্বেলের ফলকের ওপর শির-টানা দাগের মতো।
“আচ্ছা ফকির, একটা কথা বল তো আমাকে, কানাই বলল।
“কী?”
“তুই তো বলছিস ভয় পেয়েছিস। তা হলে ওখানে কেন যেতে চাইছিস?”
“মা আমাকে বলেছিল এ জায়গাটায় এসে ভয় না পেতে শিখতে হবে। এখানে যদি কেউ একবার ভয় পায় তা হলে তার দফা রফা,” বলল ফকির।
“সেইজন্যে এসেছিস তুই এখানে?”
“কে জানে,” ঠোঁট ওলটাল ফকির। তারপর একটু হেসে বলল, “এবার আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব কানাইবাবু?”
বলতে বলতে মুখের হাসি চওড়া হল ফকিরের। দেখে কানাইয়ের মনে হল নিশ্চয়ই কিছু একটা রসিকতার কথা বলবে। “কী?”
“আপনার মনটা কি পরিষ্কার, কানাইবাবু?”
চমকে উঠে বসল কানাই। “মানে? কী বলতে চাস?”
ফকির কাঁধ ঝাঁকাল : “মানে, বলতে চাইছিলাম, আপনি মানুষটা কি ভাল?”
“আমার তো তাই মনে হয়,” কানাই বলল। “অন্তত আমি যা করি তা ভাল ভেবেই করি। বাকিটা–কে জানে।”
“কিন্তু আপনার কখনও সেটা জানতে ইচ্ছে করে না?”
“সে কি কখনও কেউ জানতে পারে?” ..
“আমার মা কী বলত জানেন? বলত, এই গর্জনতলায় এসে মানুষ যা জানতে চায়, বনবিবি তা-ই তাকে জানিয়ে দেন।”
“কী করে?”
আবার ঠোঁট ওলটাল ফকির। “মা এরকম বলত।”
নৌকোটা দ্বীপের কাছাকাছি পৌঁছতেই বনের চাঁদোয়া ছিঁড়ে এক ঝাঁক পাখি ডানা মেলল। বাতাসে ভাসা মেঘের মতো খানিক চক্কর কেটে আবার গিয়ে বসল গাছে। বাদাবনের গাছের পাতার মতো পান্না-সবুজ একটা টিয়ার ঝক। এক সঙ্গে দলটা যখন উড়ল, মুহূর্তের জন্যে মনে হয়েছিল হঠাৎ যেন গাছের মাথার সবুজ কেশর ফুলে উঠেছে, দমকা হাওয়ায় আলগা হয়ে গেছে জঙ্গলের পরচুলা।
পাড়ের কাছাকাছি এসে গতি বেড়ে গেল নৌকোর। দাঁড়ের শেষ টানের সাথে সাথে ডিঙির মাথাটা গিয়ে কাদার গভীরে গেঁথে গেল। মালকোঁচা মেরে পাশ দিয়ে নেমে পড়ল ফকির। তারপর পাড়ের দিকে দৌড় দিল, ছাপগুলোকে কাছ থেকে ভাল করে দেখার জন্যে।
“আমি ঠিকই বলেছিলাম,” কাদার ওপর হাঁটু গেড়ে বসতে বসতে বলল ও। গলার স্বরে জয়ের আনন্দ। “একেবারে টাটকা দাগ। এই ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হয়েছে।”
কানাইয়ের কিন্তু এখনও একই রকম আকৃতিহীন মনে হল গর্তের মতো ছাপগুলোকে। বলল, “আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না।”
“দেখবেন কী করে?” নৌকোর দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে হাসল ফকির। “অনেক দূরে আছেন তো আপনি। ডিঙি থেকে নেমে আসতে হবে। এখানে এসে একবার ভাল করে নজর করুন, দেখতে পাবেন কেমন সোজা জঙ্গলের দিকে উঠে গেছে খোঁচগুলো,” পাড়ের ঢাল বরাবর ইশারা করল ফকির। ঢালটার ওপরে খাড়া হয়ে আছে বাদাবনের পাঁচিল।
“ঠিক আছে, আমি আসছি।” লাফ দেওয়ার জন্য কানাইকে তৈরি হতে দেখে বারণ করল ফকির : “দাঁড়ান দাঁড়ান। আগে প্যান্টটা গুটিয়ে ফেলুন, তারপর চটিটা খুলে রেখে নামুন। নইলে কাদায় চটি হারিয়ে যাবে। খালি পায়ে নামাই ভাল।”
চটিগুলো পা থেকে ছুঁড়ে ফেলে কানাই হাঁটু অবধি গুটিয়ে নিল প্যান্টটাকে। তারপর নৌকোর পাশ দিয়ে পা ঝুলিয়ে নেমে পড়েই ডুবে গেল কাদায়। শরীরের ওপরের অংশটা হুমড়ি খেয়ে এগিয়ে গেল সামনের দিকে, ডিঙিটাকে ধরে কোনওরকমে টাল সামলাল কানাই : এই কাদার মধ্যে এখন পড়ে গেলে আর মুখ দেখানোর জায়গা থাকবে না। খুব সাবধানে ডান পা-টাকে কাদা থেকে বের করে এনে একটু সামনের দিকে ফেলল। এরকম করে বাচ্চাদের মতো পা ফেলতে ফেলতে কোনওরকম দুর্ঘটনা ছাড়াই শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল ফকিরের কাছে।
“দেখুন,” মাটির দিকে ইশারা করল ফকির। “এই যে, এইগুলো নখের দাগ, আর এইখানটা থাবা।” তারপর মুখ ঘুরিয়ে ঢালটার দিকে দেখাল : “আর ওই দেখুন, এই দিকটা দিয়ে গেছে জানোয়ারটা, ওই গাছগুলোর পাশ দিয়ে। হয়তো এখনও দেখছে আপনাকে।”
ফকিরের গলার ঠাট্টার সুরটা গায়ে লাগল কানাইয়ের। ও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, “তুই কী করতে চাইছিস ফকির? ভয় দেখাতে চাইছিস আমাকে?”
“আপনাকে ভয় দেখাব?” ফকির হাসল। “কিন্তু ভয় পাবেন কেন আপনি? বলেছি না আমার মা কী বলেছিল? মন যার পরিষ্কার তার এখানে কোনও ভয় নেই।”
তারপর হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে কাদার ওপর দিয়ে নৌকোর দিকে চলল ফকির। ডিঙির কাছে গিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিল ছইয়ের মধ্যে। তারপর আবার যখন সোজা হয়ে দাঁড়াল, কানাই দেখল ফকির ওর দা-টা বের করে নিয়ে এসেছে ছইয়ের ভেতর থেকে।
দায়ের ধারালো দিকটা হাতে ধরে ফকির ওর দিকে এগোতে শুরু করতেই, নিজের অজান্তেই কেমন কুঁকড়ে গেল কানাই। চকচকে অস্ত্রটার দিক থেকে চোখ তুলে জিজ্ঞেস করল, “ওটা আবার কীসের জন্যে লাগবে?”
“ভয় পাস না,” বলল ফকির। “জঙ্গলে ঢুকতে গেলে এটা লাগবে। এই পায়ের ছাপগুলো যার, তাকে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা সেটা একবার দেখবি না?”
পেশার অভ্যেস হল গিয়ে কঁঠালের আঠা। এই অস্বস্তিকর পরিবেশেও তাই লক্ষ না করে পারল না কানাই–ওকে আপনি ছেড়ে তুই বলতে শুরু করেছে ফকির। এতক্ষণ ও-ই ফকিরকে তুই বলে সম্বোধন করছিল, কিন্তু দ্বীপে পা দেওয়ার পর হঠাৎই যেন উলটে গেছে কর্তৃত্বের সব হিসাব কেতাব।
সামনে বাদাবনের জটপাকানো দুর্ভেদ্য দেওয়াল। সেদিকে তাকিয়ে কানাইয়ের মনে হল এর ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করাটা নিছক পাগলামি হবে। ফকিরের হাত থেকে দা-টা ফসকে যেতে পারে, যে-কোনও সময়ে যা খুশি হয়ে যেতে পারে। অকারণে এতটা ঝুঁকি নেওয়া আদৌ বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।
“না ফকির, আর এই খেলা আমি খেলতে চাই না তোর সঙ্গে। এবার আমাকে ভটভটিতে নিয়ে চল,” কানাই বলল।
“কেন রে?” ফকির হেসে উঠল। “ভয় কেন পাচ্ছিস? বলেছি না, এখানে তোর মতো লোকের ভয় পাওয়ার কিছু নেই?”
কাদার মধ্যে এগিয়ে গেল কানাই। মুখ ফিরিয়ে চেঁচিয়ে বলল, “বন্ধ কর তোর উলটোপালটা বুকনি। তুই কচি খোকা হতে পারিস, কিন্তু আমি–”
হঠাৎ কানাইয়ের মনে হল পায়ের নীচে যেন জ্যান্ত হয়ে উঠেছে মাটি, টেনে ধরতে চাইছে ওর গোড়ালি। নীচে তাকিয়ে দেখল দড়ির মতো কী যেন জড়িয়ে ধরেছে দু’পায়ের গোড়ালিতে। বুঝতে পারল শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। টাল সামলানোর জন্যে মাটির ওপর পা ঘষড়ে একটু এগোতে গেল, কিন্তু মনে হল পা দুটো যেন বশে নেই। পড়ে যাওয়াটা আটকানোর জন্যে আর কোনও চেষ্টা করার আগেই থকথকে ভিজে কাদা সপাটে আছড়ে পড়ল মুখের ওপর।
পড়ে যাওয়ার পর প্রথমটায় নড়াচড়ার ক্ষমতা একেবারে লোপ পেয়ে গেল কানাইয়ের। মনে হল কেউ যেন ওর শরীরটাকে একটা ছাঁচ তৈরি করার প্লাস্টারের গামলার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। মুখ তুলে তাকানোর চেষ্টা করতে গিয়ে দেখল চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না, সানগ্লাসের ওপর কাদা লেপ্টে গিয়ে কানামাছি খেলার পট্টির মতো হয়ে গেছে সেটা। হাতের পেছন দিক দিয়ে মুখ থেকে খানিক কাদা চেঁছে ফেলে মাথার ঝাঁকুনিতে খুলে ফেলে দিল সানগ্লাসটা। চোখের সামনে সেটা আস্তে আস্তে ডুবে গেল কাদার মধ্যে। কাঁধের ওপর ফকিরের হাতের ছোঁয়া লাগতে এক ঝটকায় সরিয়ে দিল হাতটাকে। তারপর পায়ে চাপ দিয়ে নিজে নিজে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল। কিন্তু তলতলে মসৃণ কাদা শরীরটাকে চোষকের মতো টেনে ধরল, তার টান ছাড়িয়ে কিছুতেই উঠতে পারল না কানাই।
মুখ তুলে দেখল ফকির হাসছে ওর দিকে তাকিয়ে। “আগেই বলেছিলাম, সাবধান হতে।”
হঠাৎ যেন রক্ত চড়ে গেল কানাইয়ের মাথায়। স্রোতের মতো মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল অশ্রাব্য গালাগাল : “শালা বাঞ্চোৎ, শুয়োরের বাচ্চা।”
লুকিয়ে থাকা আদিম কোনও প্রবৃত্তির আগ্নেয়গিরি থেকে লাভাস্রোতের মতো বের হয়ে এল শব্দগুলো; যে উৎস থেকে সে স্রোতের উৎসারণ, কানাই নিজে কখনওই তার অস্তিত্ব স্বীকার করবে না : দাসের প্রতি প্রভুর সন্দেহ, জাত্যভিমান, গ্রামের মানুষের প্রতি শহুরে মানুষের অবিশ্বাস আর গ্রামের প্রতি শহরের বিদ্বেষ। কান্নাইয়ের ধারণা ছিল অতীতের এই সব তলানি থেকে নিজেকে মুক্ত করে ফেলেছে ও, কিন্তু যে উগ্রতায় এখন তার উৎক্ষেপণ ঘটল তাতে স্পষ্ট বোঝা গেল মুক্তি তো ঘটেইনি, তার বদলে আসলে আরও গাঢ় হয়ে জমে উঠেছে সে বিষ, জমাট বেঁধে পরিণত হয়েছে মারাত্মক বিস্ফোরকে।
কানাই নিজেও বহু বার দেখেছে এরকম, যখন ওর মক্কেলরা মেজাজ হারিয়ে ফেলেছে, প্রচণ্ড রাগের বশে লঙ্ঘন করে গেছে ব্যক্তিসত্তার সীমা, ক্রোধে আত্মহারা হয়ে ইংরেজিতে যাকে বলে ‘বিসাইড দেমসেলভস’, সেরকম হয়ে গেছে–আক্ষরিক ভাবেই। শব্দগুলোর অর্থটা একেবারে খাপে খাপে মিলে যেতে দেখেছে কানাই এই সব ক্ষেত্রে : আবেগের তীব্রতা যেন তাদের গায়ের চামড়ার শরীরী সীমা ছাপিয়ে উপচে পড়েছে বাইরে। এবং কারণ যাই হোক না কেন, প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাদের ক্রোধের লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে কানাই : দোভাষী কানাই, সংবাদবাহক কানাই, লিপিকর কানাই। দুর্বোধ্যতার খরস্রোতে ওই তাদের ভাসিয়ে রেখেছে রক্ষাকর্তা হয়ে, ফলে তাদের মনে হয়েছে চারপাশের সব কিছুর অর্থহীনতা যেন কানাইয়েরই ত্রুটি, কারণ তাদের সামনে ও-ই এক এবং একমাত্র বস্তু যার কোনও একটা নাম আছে। কানাই তখন নিজেকে বুঝিয়েছে যে এই ক্রোধোদগীরণের অধ্যায়গুলি প্রোফেশনাল হ্যাঁজার্ড ছাড়া কিছু নয়, সব পেশার সঙ্গেই যেমন কিছু কিছু অসুবিধা কি ঝঞ্ঝাট জড়িয়ে থাকে সেরকম; এর মধ্যে ব্যক্তিগত আক্রোশের কিছু নেই, পেশার খাতিরেই শুধু দুজ্ঞেয় জীবনের হয়ে মাঝে মাঝে প্রক্সি দেওয়ার কাজ করতে হচ্ছে ওকে। তবুও, এই ঘটনার সম্পূর্ণ কার্যকারণ জানা থাকা সত্ত্বেও, কিছুতেই এখন নিজের মুখ থেকে বেরিয়ে আসা কটুবাক্যের স্রোত রোধ করতে পারল না কানাই। কাদা থেকে উঠতে সাহায্য করার জন্য ফকির যখন হাত বাড়িয়ে দিল, এক ঝাঁপটায় ও সরিয়ে দিল হাতটাকে: “যা শুয়োরের বাচ্চা, বেরিয়ে যা এখান থেকে!”
“ঠিক আছে,” ফকির বলল, “তাই হোক তা হলে।”
মাথাটা একটু তুলে ফকিরের চোখদুটো এক ঝলক দেখতে পেল কানাই; আর তারপরেই, হঠাৎ যেন মুখের কথা শুকিয়ে গেল ওর। পেশাগত জীবনে দোভাষীর কাজ করতে গিয়ে এক এক বার মুহূর্তের জন্যে কানাইয়ের মনে হয়েছে যেন ও নিজের শরীর ছেড়ে অন্য লোকের শরীরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। আর প্রত্যেক বারেই যেন অদ্ভুত ভাবে বদলে গেছে ভাষা নামের যন্ত্রটার ভূমিকা। যা ছিল একটা বেড়ার মতো, একটা আড়াল-করা পর্দার মতো, সেই ভাষাই যেন হঠাৎ হয়ে গেছে স্বচ্ছ একটা আবরণ, একটা কাঁচের প্রিজম। অন্য আরেক জোড়া চোখের ভেতর দিয়ে তখন ও দেখেছে বাইরেটাকে, অন্য আরেক জনের মনের ভেতর দিয়ে জগৎটা এসে পৌঁছেছে ওর কাছে। এই অভিজ্ঞতাগুলি সব সময়েই হয়েছে খুব আকস্মিকভাবে, কোনও বারই আগে থেকে কিছু আঁচ করতে পারেনি কানাই; কোনও কার্যকারণ সম্পর্কও কিছু খুঁজে পায়নি। কেবল একটা বিষয় ছাড়া আর কোনও সাদৃশ্যের সূত্রও নেই ঘটনাগুলির মধ্যে সে সাদৃশ্য হল, এই প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই কারও না কারও সঙ্গে দোভাষী হিসেবে কাজ করছিল কানাই। এখানে যদিও ও দোভাষীর কাজ করছে না এখন, তবুও ফকিরের দিকে তাকাতেই হঠাৎ সেই অনুভূতিটা আবার ফিরে এল কানাইয়ের মনে। মনে হল যেন ওই অস্বচ্ছ ভাবলেশহীন চোখদুটোর মধ্যে দিয়ে প্রতিসারিত হয়ে যাচ্ছে ওর দৃষ্টি, আর সামনে যাকে দেখতে পাচ্ছে সে ওর নিজের চেহারা নয়, তার বদলে সেখানে রয়েছে অনেকগুলো মানুষ–যারা বাইরের পৃথিবীর প্রতিভূ, যে মানুষগুলো একদিন ছারখার করে দিয়েছিল ফকিরের গ্রাম, ওর ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছিল, খুন করেছিল ওর মাকে। কানাই এখানে সেই মানুষগুলোর প্রতিনিধি যাদের ওপর এক কানাকড়িও বিশ্বাস নেই ফকিরের মতো লোকেদের, এরকম মানুষের মূল্য ওদের কাছে একটা জানোয়ারের চেয়েও কম। নিজেকে এ ভাবে দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারল কানাই কী কারণে ওর মৃত্যু কামনা করতে পারে ফকির, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝতে পারল যে ব্যাপারটা ঠিক সেরকম নয় আসলে। ওর মৃত্যু চায় বলে ফকির ওকে এখানে নিয়ে এসেছে তা নয়, ফকির ওকে এখানে এনেছে যাচাই করার জন্যে।
হাত দিয়ে চোখের থেকে কাদা মুছল কানাই। তারপর আবার যখন তাকাল, দেখল ওর দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেছে ফকির। হঠাৎ কী মনে হতে কানাই ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে দেখার চেষ্টা করল। কাদার মধ্যে হাঁকুপাকু করে কোনওরকমে মুখটা ফেরাতেই দেখতে পেল আস্তে আস্তে নদীর মধ্যে নেমে যাচ্ছে ফকিরের ডিঙি। এখান থেকে ফকিরের মুখ দেখতে পাচ্ছিল না কানাই, ওর পিঠের দিকটা শুধু দেখা যাচ্ছিল; প্রাণপণে দাঁড় টেনে চলেছে নৌকোর পেছন দিকে বসে।
“ফকির, দাঁড়া,” চেঁচিয়ে ডাকল কানাই, “আমাকে এখানে ফেলে যাস না।”
কিন্তু দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে, একটা বাঁকের মুখ ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেছে ফকিরের ডিঙি।
ডিঙির ধাক্কায় জেগে ওঠা ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে ছিল কানাই, দেখছিল আস্তে আস্তে নদীর বুক জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে জলের স্রোত। হঠাৎ ওর চোখে পড়ল একটা তিরতিরে দাগ, কোনাকুনি এগিয়ে আসছে জলের ওপর দিয়ে। দাগটার দিকে ভাল করে নজর করতেই পরিষ্কার বোঝা গেল জলের নীচে কিছু একটা আছে ওখানে। ঘোলা জলের আবছায়া অন্ধকারের আড়ালে সেটা সোজা এগিয়ে আসছে পাড় লক্ষ করে–কানাইয়ের দিকে।
হঠাৎ ভাটির দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা নানা মরণফঁদের কথা ভিড় করে এল কানাইয়ের মনে। লোকে বলে বাঘের হাতে পড়লে নাকি পলক ফেলতে না ফেলতে প্রাণ বের হয়ে যায়, থাবার এক ঝাঁপটে ঘাড় মটকে গিয়ে সাঙ্গ হয়ে যায় ভবলীলা। যন্ত্রণা হওয়ার কোনও সুযোগই থাকে না। অবশ্য থাবার ঘা-টা আসার আগেই নাকি প্রচণ্ড গর্জনে বাহ্যজ্ঞান লোপ পেয়ে প্রাণ হারায় মানুষ। এর মধ্যেও করুণার ছোঁয়া একটা রয়েছে, অস্বীকার করার উপায় নেই–অন্তত লোকে তো তাই ভাবে। আর সে জন্যেই তো যে মানুষগুলোকে জীবনভর বাঘের সাথে ঘর করতে হয়, তাদের কাছে বাঘ শুধু একটা জানোয়ার মাত্র নয়, তার চেয়েও বেশি কিছু। পরভাষী এই দুনিয়ায় বাঘই তো একমাত্র প্রাণী দুর্বলের প্রতি যার কিছুটা হলেও একটু মায়াদয়া আছে।
নাকি কুমিরের হাতে প্রাণ যাওয়ার বীভৎস যন্ত্রণার কথা জানে বলেই এরকম মনে করে ভাটির দেশের মানুষ? কানাইয়ের মনে পড়ে গেল নদীর পাড়ের কাছাকাছিই থাকতে ভালবাসে কুমিরেরা। যে গতিতে মানুষ ঘাসের ওপর দিয়ে ছুটতে পারে, কাদার ওপর তার চেয়ে বেশি গতিতে চলার ক্ষমতা রাখে এই সরীসৃপ। পায়ের পাতা চামড়ায় জোড়া আর বুক-পেট মসৃণ হওয়ার জন্যে তলতলে পাঁকের ওপর দৌড়তে কোনও অসুবিধাই হয় না ওদের। লোকে বলে শিকার নিয়ে জলের নীচে তলিয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত তাকে নাকি বাঁচিয়ে রাখে কুমির। ডাঙার ওপর কাউকে মারে না এ জানোয়ার। শ্বাস প্রশ্বাস চালু থাকা অবস্থাতেই শিকারকে টেনে নিয়ে যায় জলের ভেতর। কুমিরে যাদের মারে তাদের শরীরের এতটুকু চিহ্নও পরে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।
কানাইয়ের মন থেকে আর সমস্ত চিন্তা মুছে গেল। কোনওরকমে উবু হয়ে উঠে পিছু হঠতে লাগল আস্তে আস্তে। মাটি থেকে উঠে থাকা ছুঁচলো শেকড়ে ছড়ে গেল সারা গা, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে উঁচু পাড়ের দিকে পেছোতে থাকল কানাই। বেশ খানিকটা পিছিয়ে যাওয়ার পর কাদা কমে এল। শুলোগুলো এখানে বেশি লম্বা, সংখ্যায়ও অনেক বেশি। জলের ওপর সেই তিরতিরে দাগটা আর দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। নদী থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে যেতে চায় এখন ও।
খুব সাবধানে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল কানাই। এক পা সামনে এগোতেই তীব্র একটা যন্ত্রণায় প্রায় অবশ হয়ে গেল পায়ের পাতাটা। মনে হল যেন একটা পেরেকের ছুঁচোলো মুখের ওপর পা পড়েছে, কিংবা একটা ভাঙা কাঁচের টুকরো মাড়িয়ে দিয়েছে ভুল করে। পা টেনে তুলতেই চোখে পড়ল কাদার গভীর থেকে মাথা বের করে রয়েছে একটা শুলো। বর্শার মতো তীক্ষ্ণ তার ডগাটা। ঠিক তার ওপরেই পা-টা ফেলেছিল কানাই। ভাল করে তাকিয়ে দেখল চারপাশের সমস্ত জায়গাটা ভর্তি হয়ে আছে ছুচোলো শুলোয়। লুকোনো ফাঁদের মতো সব ছড়িয়ে রয়েছে চতুর্দিকে। যে শেকড়গুলো এদের জুড়ে রেখেছে, এই শ্বাসমূলগুলোকে, কাদার ওপরের স্তরের ঠিক নীচে বিছিয়ে রয়েছে সেগুলো–ফাঁদের সঙ্গে জোড়া লুকোনো সুতোর মতো।
সামনেই শুরু হয়েছে বাদাবনের দুর্ভেদ্য প্রাচীর। নৌকো থেকে দেখে যেটাকে জটিল, দুর্গম মনে হচ্ছিল, সে বনকেই এখন মনে হল বিপদের আশ্রয়। এই অজস্র শুলোর মাইনফিল্ডের মধ্যে দিয়ে কোনও রকমে পথ করে সেই ঘন সবুজ জঙ্গলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল কানাই।
বাদাবনের গাছের ট্যারাব্যাঁকা সব ডালপালা এমনই লগবগে যে দু’হাতে ঠেলে সরালেও মচকে যায় না সেগুলো, ছেড়ে দিলেই চাবুকের মতো ছিটকে ফিরে আসে নিজের জায়গায়। কানাইকে যেন ঘিরে ধরল গাছগুলো, মনে হল যেন ছাল-বাকলে মোড়া শত শত হাতের আলিঙ্গনের ভেতরে এসে পড়েছে ও। গাছপালা এত ঘন যে সামনে এক মিটার দূরেও কিছু দেখতে পাচ্ছিল না কানাই। নদীটাও চোখের আড়ালে চলে গেছে। পায়ের তলায় মাটির ঢালটা না থাকলে জলের দিকে এগোচ্ছে না তার থেকে দূরে যাচ্ছে সেটা পর্যন্ত বুঝতে পারত না কানাই। এক সময় হঠাৎ করে যেন শেষ হয়ে গেল জঙ্গলের ঘন বেড়া। সামনে ঘাসে ঢাকা ভোলা একটা জায়গা। তার এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বড় বড় কিছু গাছ আর তাল জাতীয় গাছ কয়েকটা। কানাই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। সারা শরীর কেটে ছড়ে গেছে, জামাকাপড়গুলোও ছিঁড়ে প্রায় ফালাফালা। মাছি এসে বসছে গায়ে, মাথার ওপর ভনভন করছে এক ঝাক মশা।
ফাঁকা জায়গাটার চারদিকে ভাল করে চেয়ে দেখারও সাহস হল না কানাইয়ের। এটাই সেই জায়গা তা হলে? এই যদি সেই দ্বীপ হয়, তা হলে কি এখানেই কিন্তু কীসের কথা ভাবছে কানাই? শব্দটা কিছুতেই মাথায় আসছে না। এমনকী ফকির যে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কী একটা বলেছিল সেটাও এক্কেবারে মনেই পড়ছে না। ভয়ের চোটে কানাইয়ের মনটা যেন ভাষাহীন হয়ে গেছে। যে ধ্বনি আর চিহ্নগুলো এক সঙ্গে মন আর বোধের মধ্যে জলকপাটের মতো কাজ করে হঠাৎ যেন অচল হয়ে গেছে সেগুলো। মাথার ভেতরটা শুধু ভেসে যাচ্ছে নির্ভেজাল অনুভূতির বন্যায়। যে শব্দগুলোর জন্যে ও হাতড়ে বেড়াচ্ছে, যে কথাগুলো এই প্রচণ্ড ভয়ের উৎস, আসল জিনিসটাই যেন তাদের জায়গা নিয়ে নিয়েছে এখন। সমস্যাটা শুধু, ভাষা বা শব্দ ছাড়া তাকে বোঝা যাবে না, উপলব্ধি করা যাবে না তার তাৎপর্য। এ যেন শুদ্ধ চৈতন্যের হাতে গড়া এক মূর্তি, যার উপস্থিতি এমনকী আসলের চেয়েও বহুগুণে প্রবল, অনেক বেশি অস্তিত্বময়।
কানাই চোখ খুলল। সামনে তাকাতেই দেখতে পেল ওটাকে। একেবারে ওর মুখোমুখি, একশো মিটারের মধ্যে। পেছনের পায়ের ওপর ভর দিয়ে বসে আছে, মাথা তুলে তাকিয়ে রয়েছে কানাইয়ের দিকে, জ্বলজ্বলে পাঙাশ চোখে ওকে দেখছে। শরীরের ওপরের দিকের লোমগুলো রোদের আলোয় সোনার মতো রং ধরেছে। পেটের দিকটা কিন্তু গাঢ়, কাদায় ঢাকা। আকারে বিশাল, কানাই যেরকম ভেবেছিল তার চেয়ে অনেকটাই বড়। চোখদুটো আর লেজের ডগাটা ছাড়া সারা শরীরে এতটুকু স্পন্দনের লক্ষণ নেই।
এতটাই ভয় পেয়ে গিয়েছিল কানাই প্রথমটায়, যে নড়াচড়া করারও শক্তি লোপ পেয়ে গিয়েছিল। একটু দম ফিরে পেয়ে কোনও রকমে উঠে বসল হাঁটুতে ভর দিয়ে, তারপর খুব ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগল ওর কাছ থেকে। জানোয়ারটার দিক থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে পিছু হটে হটে জঙ্গলের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করতে লাগল। আর পুরোটা সময় জুড়ে মোচড় খেতে থাকল প্রাণীটার লেজের ডগা। জঙ্গলের আলিঙ্গনের ভেতর ঢুকে এসে অবশেষে খাড়া হল কানাই। তারপর কাটা-খোঁচার তোয়াক্কা না করে ঘুরে দাঁড়িয়ে দু’হাতে ডালপালা সরিয়ে এগোতে লাগল। শেষ পর্যন্ত বাদাবনের দেওয়াল ভেঙে যখন নদীর ধারে পোঁছল, তখন হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল কানাই। হাতের পেছনে চোখ ঢেকে নিজেকে প্রস্তুত করার চেষ্টা করল চরম আঘাতের মুহূর্তটার জন্য–যে প্রচণ্ড আঘাতে মট করে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে ঘাড়ের হাড়গুলি।
“কানাই!” চিৎকারটা শুনে মুহূর্তের জন্যে খুলে গেল চোখদুটো। এক পলক দেখতে পেল পিয়া, ফকির আর হরেন নদীর পাড় দিয়ে দৌড়ে আসছে ওর দিকে। তারপরেই ফের হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল কাদার ওপর, অন্ধকার হয়ে গেল মাথার ভেতরটা।
আবার যখন চোখ খুলল, তখন ও ডিঙির ওপর চিত হয়ে শোওয়া। দুপুরের রোদে ঝলসে যাচ্ছে আকাশ। একটা মুখের আদল খুব ধীরে ধীরে আকার নিচ্ছে চোখের সামনে। পিয়ার মুখ। আস্তে আস্তে বুঝতে পারছিল কানাই ওর কাঁধের নীচে হাত দিয়ে তুলে বসানোর চেষ্টা করছে পিয়া।
“কানাই? আর ইউ ও কে?”
“আপনি কোথায় ছিলেন পিয়া?” জবাবে বলল কানাই। “কতক্ষণ ওই দ্বীপটায় একা . একা ছিলাম আমি।”
“মাত্র দশ মিনিট আপনি একা ছিলেন ওখানে, কানাই। ফকিরকে নাকি আপনিই ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ও তো পড়িমরি করে এল আমাদের নিয়ে যেতে, আর আমরাও যত তাড়াতাড়ি পারি গিয়ে পৌঁছলাম।”
“আমি দেখেছি পিয়া। বাঘ দেখেছি আমি।” হরেন আর ফকিরও পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখতে পেয়ে বাংলায় বলল, “ওখানে ছিল। বড় শেয়াল–আমি দেখেছি।”
মাথা নাড়ল হরেন। বলল, “না কানাইবাবু, কিছু ছিল না ওখানে। আমি আর ফকির ভাল করে দেখেছি। কিছু দেখতে পাইনি। আর, যদি কিছু থাকত আপনি তা হলে আর এতক্ষণে এখানে থাকতেন না।”
“ছিল ওখানে, আমি বলছি।” এত কঁপছিল কানাইয়ের সারা গা যে কোনও রকমে কথাগুলি উচ্চারণ করতে পারল ও। শান্ত করার জন্যে এক হাতে ওর কবজিটা ধরল পিয়া। নরম গলায় বলল, “ঠিক আছে কানাই। আর ভয় নেই। আমরা সবাই তো এখন আছি। আপনার সঙ্গে।”
কানাই জবাব দেওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু দাতে দাঁত লেগে যাচ্ছিল বারবার, শ্বাসটা যেন খালি খালি আটকে যাচ্ছিল গলার মধ্যে।
“কথা বলবেন না,” বলল পিয়া। “আমার ফার্স্ট এইড বক্সে ঘুমের ওষুধ আছে, লঞ্চে পৌঁছেই একটা দিয়ে দেব আপনাকে। আপনার এখন একটা ভাল বিশ্রাম দরকার। তারপর দেখবেন, ভাল লাগবে।”