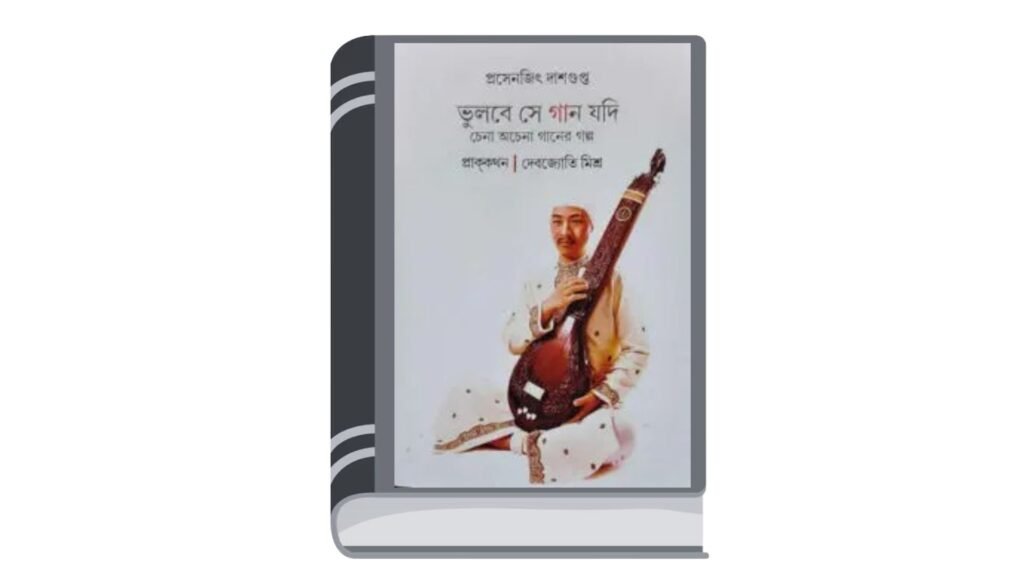ভুলবে সে গান যদি – ১০
।। দরবারীর দরবারে।।
सा रे ग_ म प ध_- नि_ सा,
सा, ध, नि, प, म प, ग, म रे सा
দরবারী। দরবারী কানাড়া। সারাজীবন যদি একটি মাত্র রাগ সঙ্গে নিয়েই নির্বাসন দেওয়া হয় আমায়, তবে আমি এই একটি রাগ নিয়েই দেশান্তরী হতে রাজি…
‘আশাবরী’ ঠাটের সেই রাগ যা অন্য কোনও রাগ না শিখেও শিখতে চেয়েছি, আত্মস্থ করতে চেয়েছি নিবিড় ভাবে। কতকটা বুঝে, কতকটা না বুঝে, সে রাগকে রাগের চাইতে বেশি মনে হয়েছে বিস্ময়। যা প্রাকৃত হয়েও অপ্রাকৃত। অদ্ভুত, ভৌতিক, অলৌকিক।
সেই রাগের সম্পর্কে বলতে গিয়ে পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ রতনঝনকর বলেছিলেন, এ পৃথিবীর সুর নয়, বুঝি বা অন্য কোনও গ্রহের। শেষ সময়ে অজানা নির্জন স্টেশনে এই রাগের হাত ধরেই অনন্তের তানপুরায় সুর বেঁধেছিলেন উস্তাদ আব্দুল করিম খান…সে আরেক গল্প।
এই সেই রাগ যার সম্পর্কে নানা জ্ঞানীগুণীজনেরা উচ্চারণ করেছেন সাবধানবানী—প্রকৃত সুর লাগাতে পারলে নেমে আসতে পারে জিন-পরি, অতৃপ্ত আত্মারা। তানসেন সৃষ্ট এই রাগকে নিয়ে কাহিনির শেষ নেই, শেষ নেই কিংবদন্তির। ভারতীয় সিনেমা-সংগীতও বঞ্চিত হয়নি এর থেকে। ‘দরবারী’ নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বহু কালজয়ী রচনা।
দীর্ঘাতিদীর্ঘ সেই তালিকা থেকে এ লেখায় তুলে নেওয়া হল একটি ‘মহারত্ন’। অসম্ভব স্বর্গীয় সেই মহার্ঘ রচনাংশ। অথচ কোথাও যেন নিঃশব্দে তার ‘স্তব্ধ’ হারিয়ে যাওয়া। আমরা তার খোঁজও রাখিনি।
১৯৫২ সাল। দেশ তখন নিতান্তই নাবালক। মানুষ স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে মাত্র পাঁচ বছর আগে। এমনই সময় মুক্তি পেল ইতিহাসবিদ রামচন্দ্র ঠাকুর-এর কাহিনি অবলম্বনে পরিচালক বিজয় ভাট-এর অমর সৃষ্টি ‘বৈজু বাওরা’। সে যুগে বা প্রথম সারির ‘মিউজিকাল ব্লকবাস্টার’।
কিংবদন্তি শাস্ত্রীয় সংগীত শিল্পী বৈজনাথ মিশ্রা ওরফে বৈজু বাওয়ার জীবনী অবলম্বনে এই সিনেমায় বিখ্যাত গীতিকার শাকিল বদাউনির কথায় সুর দিয়েছিলেন আরেক প্রণম্য সুরকার নৌশাদ। দুই মহারথীর মিশেলে সৃষ্টি হয়েছিল বহু কালজয়ী গান, যা আজও আমাদের হৃদয়ের খুব কাছাকাছি। ভারতীয় মার্গ সংগীত যার ‘সাত মহলার স্বপ্নপুরী’র স্তম্ভ।
ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে আসা বৈজু বাওয়ার মতো, সেলুলয়েডের ‘বৈজু বাওরা’ও তেমনই চর্চিত, মন্ত্রমুগ্ধতার আরেক নাম। একদিকে যেমন অভিনয়, অন্যদিকে এর সংগীত। বৈজুর ভূমিকায় ভারত ভূষণ ও তানসেনের ভূমিকায় রাজেন্দ্র-র অভিনয় আজও অবিস্মরণীয়। ঠিক তেমনই স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে এই সিনেমার কালজয়ী সংগীত। এই প্রথম কোনও সিনেমায় ‘মেইনস্ট্রিম’ আর্টিস্টও (লতা, রফি, শামসাদ বেগম)-দের পাশাপাশি ভারতীয় মার্গ সংগীতের দুই বিরল নক্ষত্রের সমাবেশ।
সেখানে সিংহভাগ দখল করে রেখেছেন উস্তাদ আমীর খান। বাকিটা ডি ভি পালুস্কর। রয়েছে অসাধারণ সব রাগের সমাহার। জনপ্রিয় গান যেমন—’তু গঙ্গা কী মৌজ’, বা ‘দুনিয়া কী রাখওয়ালে’ ইত্যাদির কথা বাদ দিলে ‘দেশী’ রাগে ‘আজ গাওত মন মেরা’, ‘মালকোষে’ নিবন্ধ ‘মন তড়পত হরি দর্শন’, পুরিয়া ধনশ্রী রাগে ‘তোরি জয় জয় করতার’ বা আমীর খানের কন্ঠে ‘মেঘ’ রাগে ‘ঘনন ঘনন ঘন’ ইত্যাদি আজও ভোলেনি সংগীতপ্রেমীরা। তবে এসব ছাপিয়েও কোথাও যেন স্বতন্ত্রতা পায় দরবারী কানাড়ায় আমীর খাঁ সাহেবের সেই অপার্থিব ‘সরগম’…
কথিত আছে (সিনেমাতেও চিত্রিত) বৈজুর বাবা গৌরীনাথ (নাম নিয়ে মতান্তর রয়েছে) ছিলেন পরম বৈষ্ণব। অনেকের মতে, তানসেনের সেই বিখ্যাত সৃষ্টি ‘মিঁয়া কী মলহার’-এর পালটা, নিজের বাবার নামে ‘গৌড় মলহার’ রাগটির রচনা করেছিলেন বৈজু। কৃষ্ণকীর্তন গেয়ে মাধুকরী ও সামান্য যজমানি করে দিন চালাতেন গৌরীনাথ। সুদূর চম্পানের (মতান্তরে চান্দেরী, গোয়ালিয়র, মধ্যপ্রদেশ) থেকে বৃন্দাবন হয়ে দিল্লি এসেছিলেন তিনি। দিল্লির রাস্তায় গান গেয়ে তিনি কৃষ্ণ নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করতেন। সঙ্গে খঞ্জনি হাতে থাকত ছোট্ট বৈজু।
এভাবেই চলছিল। কিন্তু বাধ সাধলেন সম্রাট আকবর। ‘নবরত্নসভা’র অন্যতম কিংবদন্তি গায়ক তানসেনের খ্যাতি তখন মধ্যগগনে। সারাদেশে তার মতো ‘গাওয়াইয়া’ আর দ্বিতীয় কেউ নেই। আকবর আদেশ দিয়েছিলেন—তানসেন যখন রেওয়াজে বসবেন তখন গোটা অঞ্চলে নীরবতা ও শান্তি বজায় রাখতে হবে। কোনও শব্দ করা যাবে না। করলেই দেওয়া হবে কড়া শাস্তি। কিন্তু সম্রাটের ফরমান অগ্রাহ্য করে, সেই অঞ্চল দিয়েই কীর্তন গাইতে গেছিলেন গৌরীনাথ। রক্ষীরা ছুটে এসে তাকে বারণ করলেও, তা শোনেননি তিনি। ফলত বচসা শুরু হয় উভয়পক্ষে, সেখান থেকে হাতাহাতি। রক্ষীদের প্রহারে গুরুতর জখম হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন গৌরীনাথ। মারা যাওয়ার আগে ছেলে বৈজুকে বলেন তার হত্যার প্রতিশোধ নিতে।
পিতৃশোক ‘পাগল’ (বাওরা) হয়ে যান বৈজু। সব রাগ গিয়ে পড়ে তানসেনের ওপর। তানসেনের জন্যই সে বাবাকে হারিয়েছে। তানসেন একজন ‘হত্যাকারী’ তাই তার বেঁচে থাকার অধিকার নেই। এরপর যে ভাবেই হোক তানসেনকে হত্যা করার উপায় ভাবতে থাকে বৈজু। কিন্তু পেরে ওঠে না। সময় ঘুরতে থাকে।
ক্রমে বড়ো হয় বৈজু। কিন্তু প্রতিশোধ নেওয়ার কথা ভোলেনি সে। অবশেষে একদিন মেলে সুযোগ। তানসেন তখন রেওয়াজে বসেছেন। খোলা তরবারি হাতে সেখানে উপস্থিত হয় বৈজু। উদ্দেশ্য এক কোপে তানসেনকে দ্বিখণ্ডিত করা। কিন্তু ঠিক তখনই হয় এক ‘ম্যাজিক’। এক অদ্ভুত রাগ ধরেন তানসেন। সে রাগের এমন গভীরতা, যা আচ্ছন্ন করে বৈজুকে। সারা শরীরে তার রোমাঞ্চ হয়। যেন সারা শরীরের রক্ত জমাট বেঁধে আসে। এমনই ভয়ংকর সুন্দর সে রাগ। রাগ দরবারী কানাড়া। হাত থেকে তরবারি খসে পড়ে তার। তানসেন-বধ অধরাই রয়ে যায়। পরে তানসেন নিজেই বৈজুকে বলেছিলেন, তাকে মারতে হলে তরবারি নয়, সংগীত দিয়ে যেন মারা হয়। তার গোটা জীবন সংগীতের দান। একমাত্র সংগীতই পারে তা ছিনিয়ে নিতে। পরবর্তী ইতিহাস আমাদের সকলেরই জানা।
‘বৈজু বাওরা’তে তানসেনের কন্ঠে দরবারী কানাড়া রাগের সেই সরগম সার্থকতা পেয়েছিল আমীর খাঁ সাহেবের কন্ঠমাধুর্যে। আমরা কেউ তানসেনকে শুনিনি, কিন্তু আমীর খাঁ-কে শুনেছিলাম। দরবারীর সেই অসম্ভব ‘অপ্রাকৃতিক’, স্বর্গীয় সরগম অলক্ষ্যে কোথাও মিলিয়ে দিয়েছিল ভারতীয় মার্গ সংগীতের দুই পৃথক কালখণ্ডের প্রাতঃস্মরণীয় কিংবদন্তিকে। কিন্তু সেই সুর আমরা কতটাই বা আত্মস্থ, মর্মস্থ করতে পেরেছি! চুপিসারে, অনাদরে হারিয়েছে তা। কালের গর্ভে লীন হয়েছে নিঃশব্দে, সকলের অজ্ঞাতে।
।। পাগলা সানাই।।
সত্তর দশক। পুরানী দিল্লি। সদর বাজার অঞ্চলে একটু একটু করে নামছে ভোর। শীতের সময়, তাই কুয়াশার চাদর তখনও কাটেনি পুরোপুরি। ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়তে একটু দেরি। ঈদগাহ রোডের চন্দ্র কুটিরের দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে পথচলতি মানুষেরা। কিসের যে অপেক্ষা। এমন সময় ভেসে আসে সানাই। অপার্থিব সুরে। ভৈরবীর রেশ দমকে ওঠে দিল্লির বাতাসে। অঞ্চলবাসী জানে, রেওয়াজে বসেছেন জগদীশ। বিখ্যাত সানাই বাদক জগদীশপ্রসাদ কামার। বড়ো গুণী মানুষ। তার বাবা দীপচাঁদ ছিলেন সেই জমানার আরেক প্রখ্যাত সানাইবাদক ও শাস্ত্রীয় সংগীত বিশারদ। বাবার সেই ঐতিহ্য বয়ে নিয়ে চলেছেন জগদীশ। তার সানাইয়ের মূর্চ্ছনা না শুনে ভোর শুরু হয় না এই পাড়ায়।
প্রতিদিন বাবার রেওয়াজ শুনে সেই ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠা অভ্যাস ছোট্ট মেয়েটির। চন্দ্র কুটিরের সবচেয়ে ছোটো সদস্য সে। রাতের বেলায় জন্মেছিল বলে, আদর করে জগদীশের প্রবাদপ্রতিম গুরুজি সানাই-সরতাজ উস্তাদ বিসমিল্লাহ খান সাহেব নাম রেখেছিলেন বাগেশ্বরী বা ‘বাগেশ্রী’। তার সেই নামে ছিল দেবী সরস্বতী ও ভারতীয় রাগ-রাগিনীর যৌথ সমন্বয়। বাগেশ্বরী কামার। খান সাহেবের সাকরেদ জগদীশ কামারের মেয়ে সে।
ছোটোবেলা থেকেই সানাইয়ের প্রতি ছিল বাগেশ্বরীর দুর্নিবার আকর্ষণ। তার অন্যান্য ভাইবোনেরা যখন খেলাধূলায় মত্ত, সে চুপটি করে ঘরের এক কোণে রাখা সানাইয়ে হাত বোলাতো। সানাই-ই ছিল তার একমাত্র বন্ধু। বাগেশ্বরীর খুব ইচ্ছা বাবার মতো সেও সানাইবাদক হবে একদিন। কিন্তু বাবাকে সে কথা বলার সাহস কোনদিন হয়নি ছোট্ট মেয়েটির। বলেছিল মা’কে। রক্ষণশীল পরিবার তার। বাড়িতে সংগীতের পরিবেশ থাকলেও ঘরের মেয়েরা সংগীতচর্চা করবে, সেই কথা স্বপ্নেও ভাবা যায় না। ছোটো মেয়ের আর্জি তবু জগদীশ কামারের কানে পৌঁছে দেন তার স্ত্রী। জবাবও মেলে সঙ্গে সঙ্গেই—”লড়কিও কে লিয়ে নেহি হ্যায় ইমে কাম। পড়াই লিখাই করে, গুড্ডা-গুড্ডী লেকে খেলে ঔর শাদি, ঘরসংসার করে। মর্দোওয়ালা কাম কারনে কা কই জরুরাত নেহি।” রেগেমেগে উঠে যান বাবা। দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে সেই কথা শোনে ছোট্ট বাগেশ্বরী।
কিন্তু বাবা জগদীশ কামারের প্রত্যাখ্যানে দমে যায়নি বাগেশ্বরী। সানাই তার ধ্যান-জ্ঞান-ভালোবাসা। মায়ের সাহায্যে একটি পুরোনো সানাই জোগাড় করে সে। বাবার নজর এড়িয়ে মায়ের তত্ত্বাবধানে ঘরের এককোণে, গোপনে, নিভৃতে শুরু হয় তার সাধনা। বাবা জগদীশ কামার যা বাজান, মায়ের কাছে তা জেনে নতুন করে শেখে বাগেশ্বরী। এভাবেই গোপনে, সবার অলক্ষ্যে চলতে থাকে সানাইয়ের ক্লাস। কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। একদিন হাতেনাতে ধরা পড়ে যায় সে। সুর-সাধনাতে এতটাই বিভোর যে, বাবা কখন এসে দাঁড়িয়েছেন পিছনে, তা বুঝতেই পারেননি বাগেশ্বরী। বাবাকে দেখে লজ্জায়, ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে যায় সে। কিন্তু বাবা জগদীশপ্রসাদ তাকে বকেননি। বিস্ময়ে আপ্লুত হয়ে জড়িয়ে ধরেন মেয়েকে। অবাক হয়ে তিনি শুনেছিলেন ছোট্ট মেয়েটির সানাইয়ের ‘পুকারে’ কি ভাবে ওতপ্রোত হয়ে গেছে বেনারস ও দিল্লি ঘরানার ‘সাঁঝ’। তিনি এও বুঝতে পারেন, ‘মেয়ে’ বলে বাগেশ্বরীকে সানাই না শিখিয়ে কী ভুলটাই না করেছেন। এই প্রতিভাশালী মেয়েই তার সুযোগ্য উত্তরাধিকারিনী। মেয়েকে বুকে টেনে চোখের জল মুছে তাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করেন জগদীশপ্রসাদ। সেদিন থেকে শুরু হয় নতুন করে তালিম। এরপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি বাগেশ্বরী কামারকে।
বাবা জগদীশপ্রসাদের কাছে সানাইয়ের প্রাথমিক পাঠ শেষ হলে মেয়েকে তিনি নিয়ে আসেন বেনারসে। তার গুরু উস্তাদ বিসমিল্লাহ খান সাহেবের কাছে। স্বয়ং সানাইয়ের ঈশ্বরের কাছে তার মেয়ে তালিম নিক, এমনটাই ইচ্ছা জগদীশের। বিসমিল্লাহ তারও গুরু। তাই তিনি ছাড়া অন্য কেউ এর কদর বুঝবে না, এমনটাই ধারণা ছিল জগদীশের। প্রিয় শিষ্যের প্রস্তাব শুনে চমকে যান বিসমিল্লাহ। মেয়ে শিখবে সানাই? তা কি করে সম্ভব? এ যে চিরকাল পুরুষকেন্দ্রিক বাজনা! আজ পর্যন্ত কোনও মহিলার হাতে ওঠেনি সানাই। বিসমিল্লাহ কিছুতেই রাজি হননি। শেষে জগদীশের জেদাজেদিতে বাগেশ্বরীকে কিছু বাজিয়ে শোনানোর জন্য বলেন তিনি। কাঁপাকাঁপা হাতে বাগেশ্বরী নত মুখে সুর ধরেন। শুদ্ধ কেদার। এক মুহূর্তে ‘ম্যাজিক’। সুরের সে জাদুদে বিভোর বাগেশ্বরী খেয়ালও করেননি, তার বাবা ও গুরুজি দুজনেরই চোখে তখন জল। বাজনা শেষ হলে তাকে জড়িয়ে ধরেন বিসমিল্লাহ। আবেগরুদ্ধ কন্ঠে বলেন,—”বেটি, তুনে তো’ কামাল কর দিয়া। ইসি ঘর মে বৈঠ কর মেরা বিশ্বনাথ দর্শন হো গ্যয়া।” প্রিয়শিষ্য জগদীশকে বলেন—”মা সরস্বতী কা কৃপা হ্যায় ইস পে। বহুত দূর জায়েগী ইয়ে লড়কী।” সেদিন থেকে বাগেশ্বরী কামার হয়ে গেলেন উস্তাদ বিসমিল্লাহ খাঁ সাহেবের একমাত্র ‘গাণ্ডাবন্ধ’ মহিলা সাকরেদ।
শুরু হল নতুন করে পথচলা। খাঁ সাহেবের তালিমে ক্রমেই অন্যান্য শিষ্যদের পিছনে ফেলে দেন এই অসামান্য প্রতিভাশালী মহিলা। বিসমিল্লাহ-ই তাকে সুযোগ করে দেন তার সাথে প্রথমবার স্টেজ পারফরম্যান্সের। বেনারসের সঙ্কটমোচন মন্দিরে গুরু-শিষ্যার সেই দ্বৈত সানাইবাদন আজও ভুলতে পারেননি মহল্লাবাসীরা। কিন্তু এতটাও সহজ হয়নি সেই ‘ডুয়েট’। বিসমিল্লাহ খাঁ-র নিজের ছাত্রদের একাংশ বেঁকে বসেছিল। তির্যক কটাক্ষ ছুঁড়ে দিয়েছিল রক্ষণশীল সমাজের মাতব্বরেরা। সঙ্কটমোচন মন্দিরে সানাই বাজাবে কিনা এক মহিলা? এ যে অভাবনীয়! কিন্তু কোনও কিছুতেই দমে যাননি বিসমিল্লাহ। বাগেশ্বরীকে নিয়েই তিনি বাজাবেন এবং বাজিয়েও ছিলেন। সেই বাজনা শুনে তারপর আর কেউ কোনদিন বলতে পারেননি যে সানাই শুধু, শুধুমাত্র পুরুষদের কুক্ষিগত বিদ্যা। কারণ, এক সাধারণ মহিলা তার অসাধারণ প্রতিভা, অধ্যাবসায় ও সাধনার জোরে সে ধারণা চিরকালের মতো বদলে দিয়েছেন। ততক্ষণে এটা প্রমাণিত হয়েছে শুধু সানাই কেন, যে কোনও শাস্ত্রীয় বাদ্যযন্ত্রই কোনও জাতিধর্ম ও লিঙ্গের কুক্ষিগত নয়, প্রকৃত সাধনা, ভালোবাসা ও অধ্যাবসায় থাকলে যে কেউ তার সুযোগ্য অধিকারী হতে পারে। গুরু-শিষ্যার সে দ্বৈত বাদনের শেষে ধন্য ধন্য পড়ে গেছিল মন্দির প্রাঙ্গণে। সেদিন দর্শকদের কাছ থেকে পাওয়া ভালোবাসার প্রথম ‘নজরানা’ গুরুর হাতে তুলে দিয়েছিলেন বাগেশ্বরী। বিসমিল্লাহ গরিবগুর্বদের মধ্যে বিলিয়ে দেন সেই টাকা। হেসে বলেন—এই তার শিবপুজো।
দীর্ঘ তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে সানাইয়ের জগত দাপিয়ে বেড়িয়েছেন বাগেশ্বরী। খাঁ সাহেবের যতদিন পর্যন্ত বেঁচেছিলেন ততদিন পর্যন্ত তার কাছে নিয়েছেন তালিম। হয়ে উঠেছিলেন সে বাড়ির অন্যতম সদস্যা। দেশ জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় ধ্বনিত হয়েছে তার সানাই। দিল্লি ও বেনারস ঘরানার সার্থক সংমিশ্রণ উঠে আসতো তার বাজনায়। বাজিয়েছেন দেশবিদেশের নানান অনুষ্ঠানে। অথচ, দুর্ভাগ্যের বিষয় সংগীতের জগত কোনদিন তেমন স্বীকৃতি দেয়নি এই প্রচারবিমুখ গুণী শিল্পীটিকে। সাম্প্রতিক শাস্ত্রীয় সংগীতচর্চার আসরেও তিনি অদ্ভুতভাবে ‘ব্রাত্য’। তার নামও জানে না বর্তমান প্রজন্মের শিল্পীরা। মহিলা হয়ে সানাইবাদনের মতন ব্যতিক্রমী শিল্পে পারঙ্গম হওয়াই কি এই অভাবনীয় উপেক্ষা ও অন্তরালের কারণ, এ নিয়ে বহু তর্কবিতর্ক আজও চলে শাস্ত্রীয় সংগীতমহলে। যদিও এসব বিষয় নিয়ে আদৌ মাথা ঘামাতে রাজি নন বাগেশ্বরী। আজও দিল্লির সদর বাজার অঞ্চলে কান পাতলে শোনা যায় তার জাদু সানাইয়ের মাদকতা। আজও নিরলস প্রচেষ্টায় তার শিষ্য ও বিশেষ করে শিষ্যাদের মধ্যে বপন করে চলেছেন তার সারাজীবনের অর্জিত সাধনার ফসল। দুরদর্শনে দেওয়া তার সাক্ষাৎকারে বাগেশ্বরী জানিয়ে ছিলেন, তিনি এমনিতেও ‘নিভৃতচারিণী’। স্বামী, সন্তান, শিষ্য-শিষ্যাদের নিয়ে তার একফালি জগৎ। শুধু গুরুর দেওয়া শিক্ষা দেশের নব প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়াই তার উদ্দেশ্য।
আজও পুরানী দিল্লির অলিগলিতে রাতে হাঁটলে পথচলতি মানুষ একবার ফিরে তাকান ঈদগাহ রোডের সেই চন্দ্র কুটিরের দিকে। গভীর রাতে সেই একচিলতে, বিবর্ণ বাড়ি থেকে ভেসে আসে সানাইয়ে করুণ সুর। বাগেশ্রী কানাড়া রাগে। সেই অপার্থিব সুর সানাইয়ের মোচড়ে বুকে ক্ষত রেখে দিয়ে যায়। নীরবে, নিভৃতে কোনও অজানা বেদনার অশ্রুত সুর কখন গুমরে ওঠে রাতের দিল্লির অন্ধকারে ঘেরা গুমোট আকাশে।
অঞ্চলের মানুষরা জানে রেওয়াজে বসেছেন সানাই সম্রাজ্ঞী, জগদীশ প্রসাদ ও বিসমিল্লাহ খাঁ সাহেবের স্নেহধন্যা, প্রিয়শিষ্যা বাগেশ্বরী কামার। এই ভারত উপমহাদেশের প্রথম ও সম্ভবতঃ একমাত্র মহিলা সানাইবাদক। যার কথা আজ আর কেউ মনে রাখে না।
।। ঘোষালবাড়ির গান।।
বেনারস মানেই শিল্প, কলা, সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং সংগীতের পীঠস্থান। সেখানে অলিতে-গলিতে কান পাতলে শোনা যায় টপ্পা, ঠুংরি, দাদরা, কালোয়াতি খেয়াল। বাঙালিরা এমনিতেই সংস্কৃতি-সংগীতমনস্ক। বেনারসের বাঙালি হলে তো কথাই নেই। বেনারসের ঘোষাল বাড়ির পরতে পরতে তাই জড়িয়ে ছিল এই গান। তা যেমনি-তেমনি গান নয়, রীতিমত শাস্ত্রীয় সংগীত। পরিবারের মাথা অম্বিকা ঘোষাল-এর বাবা ছিলেন ক্লাসিকালের বড়ো সমঝদার। অন্তত ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’ সিনেমায় তেমনটি দেখিয়ে গেছেন সত্যজিৎ রায়। সত্যজিৎ দেখিয়ে ছিলেন, আমরা কিন্তু আত্মস্থ করে উঠতে পারিনি।
গল্প বলছে, বেনারসের বর্ধিষ্ণু ও বনেদি বাঙালি পরিবারের অন্যতম এই ঘোষালরা। বহুযুগ ধরে প্রবাসী। বাড়িতে নাটমন্দির আছে, দুর্গাপূজা হয়। বাড়ির বৃদ্ধ কর্তা, গোয়েন্দা কাহিনির দাপুটে ভক্ত অম্বিকা ঘোষাল। একমাত্র ছেলে উমানাথ, তার স্ত্রী ও ছোটো ছেলে রুকু ওরফে ‘ক্যাপ্টেন স্পার্ক’-কে নিয়ে কলকাতায় থাকেন। অবশ্য এই বেনারসেই পড়াশোনা উমানাথের, গল্পের ভিলেন ‘মগনলাল মেঘরাজ’ আবার তারই এক সময়কার সহপাঠী। পুজোর সময়ে সপরিবারে তারা বাড়িতে বেড়াতে আসেন। এই ঘোষাল বাড়িতেই ছিল একটি মহামূল্য সম্পদ। প্রাচীন এক সোনার গনেশ মূর্তি। নেপালের জিনিস। হিরে, চুনি, পান্নাখচিত। এই গনেশ মূর্তির রহস্যময় চুরির ঘটনা নিয়েই গোটা গল্পের জাফরি কাটা, উদ্ধারে নামে প্রদোষচন্দ্র মিত্র ওরফে ফেলুদা। এর পরবর্তী ঘটনা অবশ্য সকলেরই জানা।
তবে যে জিনিসটি সত্যজিৎ দেখালেও, আমাদের কাছে উহ্য রয়ে গেছে তা হল ঘোষাল পরিবারে শুধু গনেশই ছিলেন না, ছিলেন সরস্বতীও। সারস্বত সাধনার ভিন্ন মার্গের নিদর্শন সেখানে দেখিয়েছেন সত্যজিৎ। ঘোষাল পরিবারের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত মার্গ সংগীত। ছবির একটি দৃশ্যে ফেলুদা, তোপসে, জটায়ুকে অম্বিকাবাবুর সঙ্গে আলাপ করাতে নিয়ে যাচ্ছেন উমানাথ। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ভেসে আসে ঠুংরি। কেসরবাঈ-এর কন্ঠে ‘কাহে কো দারি’। উমানাথ জানান, তার ঠাকুরদা শাস্ত্রীয় সংগীতের বড়ো ভক্ত। একসময় গানবাজনা নিয়ে প্রচুর মেতে থেকেছেন। এখন অবশ্য একজন চাকর রয়েছে শুধু গ্রামাফোনের রেকর্ড পালটাবার জন্য।
কেসরবাঈ। কেসরবাঈ কেরকর (১৮৯২-১৯৭৭)। জয়পুর-আতারৌলি ঘরানার প্রবাদপ্রতিম গায়িকা। গোয়ায় জন্ম হলেও যার সংগীতের হাতেখড়ি হয় মহারাষ্ট্রে, কোলহাপুরে। তালিম নিয়েছেন ভাস্কর বুয়া বাখলে, আল্লাদিয়া খান, আব্দুল করিম এবং রামকৃষ্ণ বুয়া ভাজ-এর মতো কিংবদন্তিদের কাছে। কলকাতাতেও গান গেয়েছেন তিনি। এই শহরই তাকে দিয়েছিল ‘সুরশ্রী’ উপাধি। শোনা যায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন তাঁর গুণমুগ্ধ। কেসরবাঈ কেরকর-এর ভৈরবীতে বিখ্যাত ঠুংরিটি সত্যজিৎ অসামান্য দক্ষতায় এই দৃশ্যে ব্যবহার করেন। এই ছবির শেষের দৃশ্যেও কেসরবাঈকে দ্বিতীয়বার শোনা যায়।
ঘোষাল বাড়িতে শোনা যায় ঊনবিংশ শতকের আরও এক অসামান্য কৃতি গায়িকা জোহরাবাঈ আগ্রাওয়ালীকেও। ছবির একটি দৃশ্যে দেখা যায় রাতের ঘোষাল বাড়িকে। সেখানে থমথমে এক পরিবেশ। অদ্ভুত শ্বাসরোধী সেই দৃশ্য। দেখা যায় গ্রামাফোনের পাশে ধ্যানস্থ অবস্থায় বসে আছেন উমানাথের ঠাকুরদা। অশীতিপর, মুণ্ডিতকেশ, ধ্যানমগ্ন এক বৃদ্ধ। টেবিলে পড়ে আছে জোনোফন রেকর্ডস। বাতাসে ভাসছে জোহরাবাঈ-এর বিখ্যাত গজল ‘পি কো হামতুম চলো’।
সেই জোহরাবাঈ (১৮৬৮-১৯১৩) যার অধিকাংশ রেকর্ডে দেখা যায় ছোটো ছেলেকে কোলে নিয়ে এক হাতে তানপুরা ছাড়ার সেই বিস্ময়কর ছবি। আগ্রা শহরে জন্ম ও মর্দানা কন্ঠের জন্য বিখ্যাত জোহরা তালিম নিয়েছিলেন আগ্রা ঘরানার প্রবাদপ্রতিম কল্লন খাঁ, মেহবুব খান (দরস পিয়া)-এর কাছে। তাঁর কন্ঠের জাদুতে মুগ্ধ হয়েছিলেন ফৈয়াজ খান এবং বড়ে গেলাম-এর মতো কিংবদন্তিরা। জোহরাবাঈ-এর সেই গজল (পরবর্তীকালে যা গেয়েছেন মেহদি হাসানও) ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’-এর ওই দৃশ্যটিকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে যায়। আর এখানেই পরিচয় পাওয়া যায় সত্যজিতের শাস্ত্রীয় সংগীতে অসামান্য মুনশিয়ানার। আজও তা অজর, অক্ষয়, চিরকালীন।
বলে রাখা ভালো, ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’-র সংগীতের বিষয়ে আলোচনায় রেবা মুহুরি-র নাম না করলে তা অসম্পূর্ণ। ঘোষাল বাড়ির দৃশ্যে যেমন ওতোপ্রোত জড়িয়ে আছেন কেসরবাঈ, জোহরাবাঈরা; ঠিক তেমনই মছলিবাবার দৃশ্যে ‘মোহে লাগি লাগন গুরু’ বা ‘হে গোবিন্দ রাখো শরণ’ ও ‘পদঘুংরু বাধ মীরা নাচিরে’-র মতো ভজনগুলিকে বোধকরি বাঙালি দর্শকেরা কোনোদিন ভুলবে না। রেবা মুহুরি সেখানে অমরত্ব পেয়েছেন। সব মিলিয়ে ফেলুদার রহস্যরোমাঞ্চ সিরিজের এই দ্বিতীয় ভাগটি যতটা গোয়েন্দা কাহিনি হিসেবে তা সার্থক, ঠিক ততটাই লঘুশাস্ত্রীয়, গজল ও ভজনের উৎকর্ষে নিদর্শন বহন করে। তাও রেবা মুহুরি এই ছবিতে তার অসামান্য গায়ন প্রতিভার পরিচয় নতুন করে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন, উক্ত দুই গায়িকা অসামান্য কিন্তু শেষমেশ বিস্মৃতির অতলেই তলিয়ে গেছেন। সত্যজিৎ নিজস্ব ভঙ্গিতে তাদের তুলে ধরেছিলেন রহস্য কাহিনির আবহসংগীতে নেপথ্য মোড়করূপে। দুর্ভাগ্য, আমরাই চিনতে পারিনি!
।। মাস্টার মদন।।
বিনতি শুনো মোরি কানহা রে
ডিসেম্বর ২৯, ১৯৪০। কলকাতা। সেবছর অল বেঙ্গল মিউজিকাল কনফারেন্সে একেবারে চাঁদের হাঁট বসেছে। চারদিনের সেই অনুষ্ঠানে ভারতীয় মার্গ সংগীতের হেন কোনও নক্ষত্র বাকি নেই, যারা কলকাতায় আসেননি। অমৃতবাজার পত্রিকা জানাচ্ছে, সূচনাপর্বের ভার পেয়েছেন রামপুরের প্রবাদপ্রতিম উস্তাদ মুস্তাক হুসেইন খান ও অমৃতসরের উস্তাদ বিলাল মহম্মদ রবাবী-র মতো দুই বিখ্যাত খেয়াল গায়ক। গোটা অনুষ্ঠানের তদারকির ভার নিয়েছেন সরোদিয়া রাধিকামোহন মৈত্র। নক্ষত্র সমাগমের তালিকা যথেষ্ট দীর্ঘ। কে নেই সেখানে! লাহোরের উস্তাদ গুলাম আলী খান বম্বের হীরাবাঈ বর্দুকর পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর মানেকাবাঈ শিরোদকর উস্তাদ জিয়াউদ্দিন ও মইনুদ্দিন খান ও পণ্ডিত রমেশ ঠাকুর (তবলা)। রয়েছেন উস্তাদ আলী আকবর খান আনোখে লাল দক্ষিণী পণ্ডিত সুন্দরম আইয়ার আশফাক হুসেইন খান (খেয়াল) রামানুজ আয়েঙ্গার পণ্ডিত মগনলাল সরস্বতী বাঈ নাগেশরাও এবং সর্বোপরি উস্তাদ আমীর খান-এর মতো জলজ্যান্ত কিংবদন্তিরা। এতসব জ্ঞানী-গুণীজন অথচ গোটা কলকাতার নজর একজনের দিকে। শুধু একজনের দিকেই। সে মাত্র ১৩ বছর বয়সী একটা বাচ্চা ছেলে, যে কিনা তার গান শোনাতে এসেছে সুদূর শৈলশহর সিমলা থেকে। বেঙ্গল মিউজিকাল কনফারেন্সের ডাকে সেই প্রথম কোনও কিশোর গান গাইতে এল কলকাতায়। কিন্তু শুধুমাত্র দর্শকই না, সেই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বিখ্যাত শিল্পীরাও সেই ‘কাল কা ছোকরা’র গান শোনার জন্য হা-পিত্যেশ করে বসে আছেন। যদিও এসবে ভ্রূক্ষেপ নেই ১৩ বছরের সেই পাঞ্জাবি ছেলেটির, লোকে তাকে চেনে ‘মাস্টার মদন’ নামে। এসবের থেকে অনেক দূরে, সে তখন ছোট্ট এক কামরার একটি ঘরে রেওয়াজ করতে ব্যস্ত। একদিন আগেই ছিল তার জন্মদিন।
সন্ধেবেলা ‘মাস্টার মদন’-এর অনুষ্ঠান। অথচ হাঁটুর বয়সী সেই বাচ্চা ছেলেটির গান শুনতে দুপুর থেকেই আছড়ে পড়ল ভিড়। তার গান শুনতে প্রথম সারিতে বসে আছেন মুস্তাক হুসেন ওঙ্কারনাথ আমীর খান দাবীর খান বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী কে এল সেহগল সহ ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের তাবড় গুণীজনেরা। গ্রিনরুমে তখন প্রস্তুতি নিচ্ছে ছেলেটি। টেনশনে গলা শুকিয়ে যাচ্ছে তার। নার্ভ ঠিক রাখতে এক গ্লাস গরম দুধ খেল সে। কেমন যেন তার স্বাদ! তবু সেসব ভাবার সময় নেই। একটু ধাতস্থ হয়েই ধীর পায়ে সে উঠে এল স্টেজে। সামনে হাজার মানুষের ভিড়, গুণিজনের সমাহার। মনে মনে মা সরস্বতী ও নানক দেব-এর নাম স্মরণ করে সে ধরল তার গান। দেশি টোড়িতে ঠুংরি—’বিনতি শুনো মেরি’। কী অদ্ভুত তার সুর। কী সাবলীল সেই বালকের গায়কি। সাক্ষাৎ সরস্বতী যেন ভর করেছেন তার কন্ঠে। প্রতিটি চলনে গোটা হল ফেটে পড়ছে সাধুবাদে। এমন অপার্থিব গান, এমন গায়কি খুব কম শোনা যায়। সেদিন যেন কলকাতাবাসীদের আরেক দেবদর্শন হল। সে সুরের জাদুতে সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ। কিন্তু তখন অন্য, অন্য কিছু একটা হচ্ছিল বাচ্চা ছেলেটির শরীরে। এত ঘাম হচ্ছে কেন? কেন গলা জড়িয়ে আসছে তার? এ কী অদ্ভুত অস্বস্তি সারা শরীর জুড়ে। গলা যেন ছিঁড়ে পড়ছে। সারা শরীরে অদ্ভুত জ্বালা! কিন্তু আসর মাঝপথে শেষ করলে সংগীতের অপমান করা হয় যে। তাই সমস্ত কষ্ট সয়ে গান চালিয়ে গেল ছেলেটি। তার সেই শারীরিক কষ্টের কথা টেরও পেল না কেউ। একসময় শেষ হয় গান। উঠে দাঁড়িয়ে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রণাম করে সে। গোটা হল ফেটে পড়ছে হাততালিতে। সংগীতের বোদ্ধারা হারিয়ে ফেলেছেন তাদের ভাষা। শুধু নিঃশব্দে তারা করে গেলেন আশীর্বাদ। আর সেই ছেলেটি? সে তখন ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়েছে ব্যাকস্টেজে। বাথরুম পর্যন্ত যেতেও পারেনি, তার আগেই গ্রিনরুমের বাইরে দমকে দমকে বমি। যেন দেখা গেল দু-ফোঁটা রক্তের দাগও। কেন এমন হল? কেন? কেন? কেন? তবে কি আবারও সেই চক্রান্ত? আবারও সে ষড়যন্ত্রের শিকার? আবার? অচৈতন্য হওয়ার আগে ছেলেটি মনে করতে পেরেছিল—স্টেজে ওঠার আগে সেই দুধের গ্লাস, আর তার অদ্ভুত স্বাদ। তবে কি সেই দুধেই মেশানো ছিল কিছু? ঘন অন্ধকার নেমে আসে ছেলেটির চোখে। সেই অন্ধকার যা একটু একটু করে গ্রাস করছে তার বোধ, তালিম, সুর আর সত্তা। ঘন দুধের মতো জমাটবাঁধা সেই আঁধারে একটু একটু করে তলিয়ে যায় সে। গ্রিন রুমে তখন সবার অলক্ষ্যে পড়ে থাকে একটি গ্লাস। যার গায়ে তখনও লেগে দুধের গন্ধ।
ইয়ুন না রয়হ্ রয়হ্ কর হমে তরসাইয়ে
ডিসেম্বর ২৮ (মতান্তরে ২৬), ১৯২৭। পাঞ্জাবের জলন্ধর জেলার খানখানায় এক ধর্মপ্রাণ শিখ পরিবারে জন্ম মাস্টার মদনের। আকবরের নবরত্নসভার অন্যতম রত্ন, এবং একাধারে বিখ্যাত যোদ্ধা ও ইসলামী কবি-দার্শনিক আব্দুল রহিম খানখানান-এর তৈরি এই গ্রাম খানখানায় বাস করতেন সর্দার অমর সিং ও তার স্ত্রী পূরণ দেবী। তাদেরই কনিষ্ঠ সন্তান মদন সিং। মদনের থেকে ১৩ বছরের বড়ো ভাই মোহন নিজে বেহালা-বাদক ও সুদক্ষ গায়ক। দিদি শান্তিদেবীও ছিলেন সুগায়িকা। ছোটোবেলা থেকেই বাড়িতে গানের পরিবেশ। সর্দার অমর সিং সরকারি কর্মী হওয়ার সঙ্গে নিজেও ভালো গাইতেন। অঞ্চলের বিভিন্ন গুরুদ্বারা ও মন্দিরে তার ভজন ছিল বিখ্যাত। ছোটো ছেলেকে শিখিয়েছিলেন গুরু তেগবাহাদুর রচিত ‘শাহাবাদ’—’চেতনা হ্যায় তো চেত লে’। গানপাগলদের সংসারের হাল সামলাতেন পূরণদেবী। মদন এককথায় যাকে বলে চাইল্ড প্রডিজি। ছিলেন প্রবল শ্রুতিধর। যা কিছু শুনতেন তা মনে ধরে রাখার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। প্রথাগত সংগীতের তালিম মদন পেয়েছিলেন কিনা তা নিয়ে রয়েছে মতভেদ। তবে শোনা যায় তিন বছর বয়সে বিখ্যাত শাস্ত্রীয় সংগীতশিল্পী পণ্ডিত অমরনাথের কাছে তালিম নিয়েছিলেন তিনি। পণ্ডিত অমরনাথ ছিলেন সে যুগের বিখ্যাত সুরকার হুসনলাল-ভরতনাম-এর দাদা। পরে তিনি নিজে ‘মির্জা সাহিবা’ (১৯৪৭) সিনেমায় সুরারোপ করেন ও পাকিস্তানের বিখ্যাত শিল্পী নূরজাহান তাতে অসামান্য কিছু গান গেয়েছিলেন। গুরুর তালিমের পাশাপাশি মাস্টার মদন নিজেও যে অসম্ভব প্রতিভাবান ছিলেন সে নিয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না। মদনের জন্মের অল্পকিছু কালের মধ্যেই সরকারি কাজে সিমলায় বদলি হয়ে যান সর্দার অমর সিং। সিমলাতে নতুন করে শুরু হয় মদনের সংগীতচর্চা। দাদা-দিদির অকুণ্ঠ উৎসাহ ও সাহচর্যে ক্রমেই শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, ভজন, খেয়াল ও গজলে অসামান্য ‘পকড়’ তৈরি হয় তার। সে সময় সিমলাতে রেমিংটন র্যাণ্ড টাইপ রাইটার কোম্পানিতে কাজ করতেন বিখ্যাত গায়ক কে এল সেহগল। সর্দার অমর সিং-এর কোঠিতে ছিল তার নিত্য যাতায়াত। সিং পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে এলেই তিন ভাই বোনকে নিয়ে স্বরসাধনায় মাততেন সেহগল। ঘন্টার পর ঘন্টা চলত তাদের রেওয়াজ। তিন ভাই-বোনের মধ্যে অসামান্য গায়কি ও সুরের অধিকারী মদন ছিলেন সেহগলের বিশেষ প্রিয় পাত্র। তার তালিম এমনই তৈরি হয় যে মাত্র চার বছর বয়সে, ১৯৩০ সালের জুন মাসে ধরমপুর স্যানিটরিয়ামে হয় মদনের প্রথম পাবলিক অ্যাপিয়ারেন্স। গেয়ে ছিলেন ভজন, মিশ্র কাফীতে ‘হে সারদা নমনঃ করু’। প্রবল জনপ্রিয়তা পান সেই আসর থেকেই। কৃতিত্বের সম্মানরূপে পেয়েছিলেন একটি ছোট্ট সোনার মেডেল। পেলেন নতুন পরিচয়। মদন সিং থেকে হলেন ‘মাস্টার মদন’। বলাবাহুল্য মদনের সুরের জাদুতে মাত হল সিমলা। সকলের মুখে তখন একটাই নাম। ঈশ্বরের অপার কৃপা ছিল মদনের গলায়। পাঁচ বছর বয়সেই অবলীলায় তিনি গেয়ে দিতেন শক্ত শক্ত রাগ-রাগিনী, খেয়াল, ধ্রুপদ, ভজন। ক্রমেই সিমলা ছাড়িয়ে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ল মদনের নাম। ডাক আসতে থাকে বিভিন্ন শহর, রাজ্য ও নেটিভ স্টেটের রাজা-রাজড়াদের দরবার থেকেও। প্রবল জনপ্রিয়তাই পরবর্তীকালে কাল হয়েছিল তার।
মদন যেখানেই গেছেন পেয়েছেন অসংখ্য সম্মান। তার একটি ‘পসন্দিদা’ কোট ছিল, যেটা প্রায় ঢেকেই গিয়েছিল মেডেলের বন্যায়। সেই ছোট্ট কোটটি পরেই সে ঘুরে বেড়াত সারাদেশ। মদন তখন সমস্ত দেশবাসীর কাছে এক অপার বিস্ময়। যেখানেই গেছে সেখানেই কুড়িয়েছে প্রশংসা। মদনের হাত ধরেই হাল ফিরেছিল অমর সিং’-এর সংসারে। এর মধ্যেই গানের পাশাপাশি সে চালিয়ে গেছে পড়াশোনা। সেহগলেরই উৎসাহে সিমলার সনাতন ধর্ম স্কুলের গণ্ডি টপকে দিল্লি পাড়ি দিয়েছে শিল্পী। প্রথমে রামজশ স্কুল ও পরে হিন্দু কলেজে ভরতি হয় সে। কিন্তু পড়াশোনা চালাতে পারেনি বেশিদিন। অধিকাংশ সময়ে হয় রেওয়াজ, না হয় অনুষ্ঠান করতে ভারতভ্রমণ চলছিল তার। বন্ধু-বান্ধবও জোটেনি তেমন এই মুখচোরা, লাজুক ছেলেটির। মাঝেমধ্যে কলেজ ক্যান্টিনে দেখা যেত তাকে। খাবার ফেলে মাটির দিকে তাকিয়ে গুনগুন করছে সে। সামনে দুধের গ্লাস। দুধ খেতে ভালোবাসতো খুব। ওর মধ্যেই চলছে সরগম আর পালটা সাধা। রেওয়াজের প্রতি এমনই ছিল তার ডেডিকেশন। ঘনিষ্ঠজনেরা বলেন, একবার চারদিনের ‘চিল্লা’ও করেছিলেন মদন। সে বড়ো ভয়ংকর জিনিস। ‘চিল্লা’ হচ্ছে একপ্রকার কঠোর রেওয়াজের মার্গ। সারাদিনে অল্পকিছু খাওয়া ও গোসল করাটুকু ছাড়া দিনের পুরো অংশ দিতে হত রেওয়াজে। ‘চিল্লা’র কুপ্রভাব পড়ে তার স্বাস্থ্যেও। সে সময় একটি দশ-এগারো বছর বয়সের ছেলে ‘চিল্লা’ করছে ভাবলে, আচ্ছা আচ্ছা ওস্তাদেরা চোখ কপালে তুলে ফেলবেন। এর ফলেই প্রবল অসুস্থ হয়ে পড়েন মদন। কিন্তু গান বা রেওয়াজ—দুটির কোনওটি থেকেই তিনি সরে আসেননি। সরে আসছিল আসলে সময়। দ্রুত, খুব দ্রুত ফুরোচ্ছিল তা। মুছে যাচ্ছিল তা একটু একটু করে ‘চাইল্ড প্রডিজি অফ সিমলা’র জীবন থেকে। টের পাননি কেউ। কিন্তু তা ভালোই বুঝতে পেরেছিলেন মদন নিজে।
হ্যয়রত সে তাক রাহা হ্যায় জানে-ওয়াফা মুঝে
তিন দশকের শেষভাগ। ততদিনে খ্যাতির মধ্যগগনে মাস্টার মদন। মাত্র আট বছর বয়সেই মুক্তি পেয়েছে তার প্রথম গ্রামোফোন রেকর্ড। বিখ্যাত শায়ের সাগর নিজামীর লেখা দুটি গজল—’ইয়ুন না রয়হ রয়হ কর হমে তরসাইয়ে’ ও ‘হ্যয়রত সে তাক রাহা হ্যায়’ গেয়েছিলেন মদন। রীতিমতন হইচই পড়ে গিয়েছিল সর্বত্র। ওটুকু বয়সেই মদন ছুঁয়ে ফেলেন জনপ্রিয়তার শীর্ষ। কিন্তু বাধ সাধে তার ভগ্ন স্বাস্থ্য। দীর্ঘদিন হল একটুও বিশ্রাম পায়নি ছোটো ছেলেটি। সারাদেশ জুড়ে অবিশ্রান্ত ঘোরাঘুরি একটু একটু করে শেষ করে ফেলছিল তাকে। একটুতেই হাঁপিয়ে উঠতেন, তার সঙ্গে ছিল ঘুসঘুসে জ্বর আর কাশি। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তার খ্যাতির আলোয় অন্ধ হয়েছিল তার নিজের পরিবার। পাননি যত্ন, পরিচর্যা বা খাওয়া-দাওয়া। অনেকের মতে তাকে ঘিরে পরিবারের একাংশের উচ্চাকাঙ্খা ও স্বার্থপরতা ছিল তার ভগ্ন স্বাস্থ্যের অন্যতম কারণ। আর এর পাশাপাশি ছিল তার সেই সময়কার প্রতিদ্বন্দ্বীদের ঈর্ষা ও চক্রান্ত। মদন-এর ঘনিষ্টজনেরা জানিয়েছেন, তার গায়কি ও অল্পবয়সে দেশজোড়া খ্যাতি সহ্য করতে পারেননি তারই সমকালীন শিল্পীগোষ্ঠীর একাংশ। ভাবতেও অবাক লাগে, তার গান চিরতরে থামিয়ে দিতে একাধিকবার হয়েছে ষড়যন্ত্র। একবার আম্বালায় গান গাইতে গিয়ে এক তবায়েফ মাস্টার মদনকে নিজের কোঠিতে ভজন গাওয়ার আমন্ত্রণ জানান এবং তাকে বিষাক্ত একটি পান খাইয়ে দেন। অনেকের মতে, মদনকে চিরতরে সরিয়ে দিতে দিল্লির রেডিও স্টেশনেও কেউ গোপনে তার দুধে মিশিয়ে দেয় পারা। এমনকি ১৯৪০ সালে কলকাতার অল বেঙ্গল মিউজিকাল কনফারেন্সের অনুষ্ঠানের সময়েও তাকে দুধে বিষ মিশিয়ে স্লো পয়েজনিং করে মেরে ফেলার চেষ্টাও চলেছিল। কারা করেছিল এসব? কারোর মতে পরিবারের লোকজন, কারোর মতে রাইভাল মিউজিশিয়ানদেরই কেউ কেউ। কলকাতার সেই অনুষ্ঠানের পর মদনের স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি হয়। ধরা পড়ে দুরারোগ্য টিউবারকিউলোসিস। দিল্লিতে দিদির বাড়িতে থেকে তবুও তিনি নানা ঘরোয়া অনুষ্ঠান ও রেডিওতে গান গাওয়া জারি রেখেছিলেন। ১৯৪০ সালে সিমলায় তার অনুষ্ঠানে এমনই অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে, যে একই সময়ে সিমলায় আয়োজিত মহাত্মা গান্ধির একটি সভাতে দেখা যায় হাতেগোনা কিছু লোকের উপস্থিতি। এই ঘটনায় নাকি অবাক হয়ে গান্ধিজি নিজেই মাস্টার মদনের গান শোনার ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। জানা নেই, সেই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎ আদৌ বাস্তবে ঘটেছিল কিনা। কারণ, মদন নিজে তখন গুরুতর অসুস্থ, ক্ষয়রোগ ও ভেদবমির শিকার। অবশেষে দীর্ঘ রোগভোগের পর ১৯৪২ সালের ৫ জুন সিমলায় মায়ের কোলে মাথা রেখে চিরনিদ্রার দেশে পাড়ি দেয় ভারতীয় মার্গ সংগীতের বিস্ময় বালক মাস্টার মদন। পিছনে পড়ে থাকে শুধু আটটি গানের অপার ভাণ্ডার। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল মাত্র ১৪ বছর ৫ মাস। গোটা সিমলা জুড়ে বৃষ্টি হয়েছিল সেদিন। হাজার হাজার সিমলাবাসীদের চোখের জল মিশে গিয়েছিল তাতে। তাকে দাহ করার সময় তার মেডেল-খচিত কোর্টটিও তুলে দেওয়া হয় চিতায়। সেই বছরের শেষে পুত্রশোকে জর্জরিত মা পূরণদেবীও পাড়ি দেন অমৃতলোকে। মদনের বাবা সর্দার অমর সিং প্রায় ৪০ বছর পর দিল্লিতে দেহ রাখেন। ঘটনার প্রায় ৬০ বছর পর বিখ্যাত গজল গায়ক জগজিৎ সিং HMV থেকে ‘গজল কী সফর’ নামের একটি শতবার্ষিকী সংকলন সম্পাদনা করলে তাতে ঠাঁই পায় মাস্টার মদনের দুটি অবিস্মরণীয় গজল।
আজ এত বছর পর ভারতীয় মার্গ সংগীতের এই বিস্মৃত অধ্যায়টিকে স্মরণ করতে বসে বারবার অবাক হয়েছি এই ভেবে যে, মাস্টার মদনের মতো তরুণ প্রতিভাকেও কী রকম প্রতিকূলতা, হিংসা, স্বার্থপরতা ও পরিবারের উচ্চাকাঙ্খা তিলেতিলে শেষ করে দেয়। আজ থেকে এত বছর আগেও এ ধরনের ঘৃণ্য মানসিক অবক্ষয়ের পরিচয় যেন প্রতিমুহূর্তে চাবুক কষায় আমাদেরই। মাত্র ১৪ বছরেই নিভে গেল যে প্রতিভা, তার দায় শুধু পরিবারের উচ্চাকাঙ্খা বা হীন মনোবৃত্তির কিছু মানুষেরই নয়, দায় এই সমাজেরও যা মাস্টার মদন-এর মতো হাজার হাজার প্রতিভাকে সময়ের আগেই ঠেলে দেয় অপ্রত্যাশিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে। হয় জেত, না হয় হারিয়ে যাও—যার নীতি। যুগে যুগে এভাবেই সবার অলক্ষ্যে হারিয়ে যায় মাস্টার মদন-এর উত্তরসূরিরা। আমরাই পারি এইসব অকালে হারিয়ে যাওয়া আটকাতে, ফিরিয়ে আনতে সেইসব বিস্ময়কর প্রতিভাদের। তবেই অক্ষয়, শাশ্বত হবে ভারতীয় সংগীত, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের আগামী ভবিষ্যৎ।
।। শূন্য এ বুকে পাখি মোর।।
নজরুল জয়ন্তী এলেই এই গানটার কথা আজও ভীষণ মনে পড়ে। জানিনা কেন, শুধু এই গানটাই। অথচ নজরুল মানেই তো কত শত সহস্র অসাধারণ সব গান। জ্ঞান গোঁসাই, মানবেন্দ্র, ধীরেন বসু বা ফিরোজা বেগম-এর কন্ঠে অবিস্মরণীয় কত রচনা! কিন্তু না, অন্য কোনও গান নয়, শুধু এই গানটাই! হয়তো ‘ছায়ানট’ রাগটাই এমন, হয়তো এই গান ও তার কথাগুলো…জানিনা কেন মনে হয় কোনও ভাবেই তা এই পৃথিবীর নয়। অন্য কোনও নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে ভেসে আসা সেই সুর, সেই ‘সাঁঝ’ বা হৃদয় নিংড়ে উঠে আসা কিছু অপার্থিব শব্দযাপন!
তুই নাই বলে ওরে উন্মাদ/পাণ্ডুর হল আকাশের চাঁদ
এই গানকে নিয়েই একসময় কত তর্ক-বিতর্ক, অভিযোগ ও দোষারোপের পালা চলেছে। বিশারদরা মনে করেন এই গানের সূত্রপাতে রয়েছেন—রবীন্দ্রনাথ। ১৯০১ সালে তাঁর লেখা—’অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর যাহা যাহা তাহা যায়।’ সেই অনন্য ‘ছায়ানট’। বহুজনের মতে, ভাইপো নীতীন্দ্রনাথের অকালমৃত্যু ব্যাথিত করেছিল রবীন্দ্রনাথকে। তারই উদ্দেশে লেখা হয় গানটি। অনেকে মনে করেন, প্রিয় পুত্র শমীন্দ্রের মৃত্যুতে লেখা এই গান। এ নিয়ে আগেও তর্ক-বিতর্ক ছিল, এখনও রয়েছে। কিন্তু সে সময় এই গানটি প্রবল আলোড়ন ফেলেছিল জনমানসে। গানটির সুরমাধুর্যে আলোড়িত হয়েছিলেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীও। তিনি শাস্ত্রীয় সংগীতের বিরাট পথিকৃৎ। গানটিকে আরও বেশি শাস্ত্রীয় অঙ্গে গাইবার জন্য—অর্থাৎ তানকারী, আলাপ-বিস্তার সহযোগে—মনস্থ করেন। ঠিক করেন, নিজস্ব স্টাইলে গাওয়া সেই গানটি স্বয়ং ‘গুরুদেব’-কে শুনিয়ে গানটি পরিবেশন করার অনুমতি চাইবেন। সেই মতো এক পরিচিতের মাধ্যমে এল সুযোগও। মন-প্রাণ ঢেলে গান গাইলেন জ্ঞান গোঁসাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ-এর একটুও পছন্দ হয়নি। তাঁর মতে, গানটির অন্তর্নিহিত অসম্ভব যে বেদনা, হারানোকে ফিরে পাওয়ার আর্তি, জীবন দর্শন ও সর্বোপরি সুরের সেই স্থিতধী ভাব কোথাও যেন হারিয়ে গেছিল শাস্ত্রীয় রাগদারীতে। গানটির ভাব তথা সুর মাধুর্য বিঘ্নিত হয়েছে তাতে। ফলত এককথায় জ্ঞানবাবুর প্রস্তাব নাকচ করলেন তিনি।
তোর তরে বনে উঠিয়াছে ঝড়/লুটায় লতা ধূলায়
মনের দুঃখে নজরুল-এর কাছে এলেন গোঁসাই বাবু। রাখলেন আর্জি, ঠিক ওমনি একটা গান বানিয়ে দিতে হবে তাকে। কথায় ও সুরে যা রবি ঠাকুরের গানের চাইতে কোনও অংশে কম হবে না। সেই গান গেয়ে ‘গুরুদেব’-কে তাক লাগিয়ে দিতে চান জ্ঞানবাবু। হেসে ফেলেন নজরুল। বলেন, গুরুদেবের রচনার সমকক্ষ রচনা সৃষ্টির ক্ষমতা তাঁর কেন, এ দেশে কারোর নেই। তিনি চিরপ্রণম্য, অপার এক সমুদ্র যার তল মেলা ভার। কিন্তু জ্ঞান বাবু নাছোড়, ওমনিই একটা গান বেঁধে দিতে হবে তাকে, দিতেই হবে। অবশেষে রাজি হলেন নজরুল। চেয়ে নিলেন সময়। নজরুল শেষ পর্যন্ত গানটি লিখেছিলেন তাঁর পুত্র বুলবুলের অসময়ে মৃত্যুর পরে। একই ছায়ানট রাগ, অবিকল একই তার। আর কথায় যেন স্বয়ং ‘গুরুদেব’কেও ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। সৃষ্টি হল—’শূন্য এ বুকে পাখি মোর আয়, ফিরে আয়, ফিরে আয়’। জ্ঞানবাবু তা রেকর্ড করেন।
গোটা বাংলা উত্তাল হয়ে ওঠে সেই সুরে। বাংলা গানের জগতে আরও একটি ইতিহাস রচনা করলেন নজরুল। কিন্তু ঠাকুরবাড়ির ঘনিষ্ঠ অনেকেই সে সময় এই রচনাটি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এমনকি উঠে ছিল ‘সুর চুরি’র অভিযোগও। অথচ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং নজরুল-এর বিরুদ্ধে ওঠা এসব অভিযোগকে কোনওদিনই আমল দেননি। সদগুণীই গুণের কদর বোঝেন। নিন্দুকেরা এরপর এসব নিয়ে কিছু বলার সাহস পাননি।
তুই ফিরে এলে ওরে চঞ্চল/আবার ফুটিবে বন ফুল দল
‘শূন্য এ বুকে পাখি মোর’ আজও বাংলা গানের জগতে অবিসংবাদী প্রভাব রেখে চলেছে। দশকের পর দশক নজরুল-অনুরাগীরা নিজ নিজ সুরের তরণী ভাসিয়ে তাঁদের শ্রদ্ধা উজাড় করে দিয়েছেন এর প্রতিটি কথা ও সুরের চলনে। ‘ছায়ানট’ রাগের হাত ধরে বাংলা সংগীত জগতের দুই মহীরুহ, দুই ক্ষণজন্মা পুরুষ, দুই শোকার্ত পিতা—রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল কোথায় যেন সুরের পরতে মিলেমিশে এক হয়ে রইলেন। নিরাকার, অখণ্ড ব্রহ্মের মতো!
।। বনরাজ।।
১৯৭৬ সাল। গুজরাটের সেই প্রত্যন্ত প্রান্তর। দিকচক্রবালে মিশে যাওয়া রেললাইন। ছোট্ট জনপদ, প্ল্যাটফর্মবিহীন স্টেশন। আকাশ কালো করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ঢুকে পড়ছে রেলগাড়ি। গ্রামের নতুন পশু-ডাক্তার আসছেন। নেপথ্যে প্রীতি শর্মার কণ্ঠে—’মেরো গাঁও কথা পরে/যা দুধ কী নদিয়া বহে’…ঠিক এভাবেই শুরু হচ্ছে শ্যাম বেনেগলের বহুচর্চিত ‘মন্থন’। গুজরাট-রাজস্থান সীমান্ত ছুঁয়ে উঠে আসা সেই বিখ্যাত লোকগীতি। বহুজনের মতে, রাজস্থানী লোকগীতি ‘কেশরিয়া বালমে’র সমকক্ষ যদি কোনও গান থেকে থাকে তবে তা এটিই।
সাল ১৯৮১। উত্তর কলকাতা। সরু অলিগলি ধরে এগিয়ে আসছে হাতে টানা রিকশা। তাতে বসে এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বৃদ্ধা, ভায়োলেট স্টোনহ্যাম ওরফে জেনিফার কেন্ডেল। রিকশা ছেড়ে নেমে এগিয়ে যান পুরোনো কলকাতার ব্রিটিশ জমানার বাড়ির দিকে। লিফট বন্ধ। ধীর, ক্লান্ত পায়ে অন্ধকার সিঁড়ি ভেঙে উঠতে থাকেন বৃদ্ধা। নেপথ্যে পিয়ানো কনচের্তোয় উঠে আসে তার অতীত। অদ্ভুত মন-কেমন করা সুর। অপর্ণা সেন-এর ‘৩৬ চৌরঙ্গী লেন’-এর সুর সেই একাকিত্ব, নিঃসঙ্গতা ও প্রতারণার নির্মোক, উলঙ্গ চিত্রটি তুলে ধরে।
আশি দশকের মাঝামাঝি। টিভির পর্দায় আগুন ধরাচ্ছেন রঙিন ফুলছাপ শাড়ি পরিহীত লাস্যময়ী মধু সাপ্রে। ‘গার্ডেন ভরেলী’ শাড়ির বিখ্যাত সেই বিজ্ঞাপন আর ততধিক বিখ্যাত তার জিঙ্গল যা পরবর্তীকালে নতুন করে শোনা যাবে মণিরত্নমের ‘রোজা’ সিনেমায় সেই ‘রোজা জানেমন’ গানটির আবহে। এ আর রহমান নামের তরুণ এক দক্ষিণী সঙ্গীত পরিচালকের সুরে।
আশির দশকেরই শেষে ভীষ্ম সহানীর অমর রচনা অবলম্বনে গোবিন্দ নিহলানীর ‘তমস’ (১৯৮৮) মুক্তি পেল। পার্টিশান নিয়ে নির্মিত দেশের দীর্ঘতম টেলি-সিরিজ। আর সেখানেও উঠে আসছে পঞ্জাবের লোকগীতি আর স্বজনহারাদের বিষাদের মেলবন্ধনে রচিত অমোঘ সেই সুর।
এবার ১৯৯৬। দাঙ্গা কবলিত দিল্লি। বিক্ষোভকারী জনতার ছোঁড়া পাথরে রক্তাক্ত, আহত হয়ে লুটিয়ে পড়লেন ‘সরদারী বেগম’। তার শেষ সময় আগত। মেয়ে সাকিনার কাছে শুনতে চান গান। কান্নাভেজা গলায় সাকিনা গান ধরে ভৈরবীতে—’চলি পি কে নগর’…শ্যাম বেনেগালের ‘সরদারী বেগম’ যত না নির্দেশনা ও অভিনয়ের জোরে, তার চেয়ে অনেক বেশি আলোকিত হয়ে উঠলো তার সঙ্গীতের জাদু কাঠির ছোঁয়ায়।
সুদীর্ঘ চার দশক ধরে এভাবেই বলিউডে স্বতন্ত্র ও ব্যতিক্রমী স্থান ধরে রেখেছেন বনরাজ। বনরাজ ভাটিয়া। দেশের অন্যতম বিশিষ্ট ও প্রবীণ সুরকার তিনি। চার দশকে হাতেগোনা ২০-২৫টি সিনেমাতে তিনি সুর দিলেও, তার প্রগাঢ় সাঙ্গীতিক জ্ঞান, মেধা, দীক্ষা এবং যন্ত্রের উপর অসামান্য দক্ষতা, নজরকাড়া মুনশিয়ানায় বলিউডে আলাদা মান ও সম্ভ্রম কেড়ে নিয়েছিলেন বনরাজ। একসময়ে নির্দেশক শ্যাম বেনেগল-এর সার্থক এবং একমাত্র ‘জুড়িদার’ ছিলেন বনরাজ। বেনেগলের ছবি মানেই সঙ্গীতে তিনি। ‘অঙ্কুর’ (১৯৭৪), ‘জুনুন’ (১৯৭৮), ‘ভূমিকা’ (১৯৭৭), ‘মাণ্ডি’ (১৯৮৩) অথবা গোবিন্দ নিহাললীর ‘দ্রোহকাল’-এ (১৯৯৪) তাঁর সুরসংযোজন অসাধারণ। ‘সুরজ কা সাতওয়ান ঘোড়া’র ‘ইয়ে শামে’ গানটি আজও অন্যতম সেরা লাভ সং রূপে পরিচিত। এখানেই শেষ নয়। ক্লাসিক কমেডি ‘জানে ভি দো ইয়ারো’ (১৯৮৩), দেশভাগের উপাখ্যান ‘তমস’ বা বাঈজী সংস্কৃতির শেষ স্বাক্ষর ‘সরদারী বেগম’-এ (১৯৯৬) তাঁর সঙ্গীত অবিস্মরণীয়। ‘তমস’ বনরাজকে এনে দিয়েছিল জাতীয় পুরস্কারের স্বীকৃতি। এরপর একে একে তাঁর অসামান্য কীর্তির জন্য পেয়েছেন বি এফ জে অ্যাওয়ার্ড, সঙ্গীত নাটক আকাদেমী ও পদ্মশ্রীর মতো অনন্য সম্মান।
১৯২৭ সালের ৩১মে মুম্বইতে জন্মানো বনরাজ ভাটিয়া আজ ৯২ বর্ষীয় অশীতিপর বৃদ্ধ। সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে জানতে পারলাম অসহায়, একাকী, নিঃস্ব অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন লন্ডনের রয়াল অ্যাকাডেমী অফ মিউজিকের এই গোল্ড মেডেলিস্ট। বলিউডে পা রাখার আগে বহু আগে ষাট দশকে যিনি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে টানা পাঁচ বছর মিউজিক ডিপার্টমেন্টে অধ্যাপনা করেছেন, আজ তিনি নিজেই প্রতিদিন একটু একটু করে হারিয়ে যাচ্ছেন বিস্মৃতির অতল অন্তরালে। হাঁটুর ব্যথায় জর্জরিত, ধরেছে হৃদরোগ, আংশিক স্মৃতিভ্রংশ, চলা-ফেরায় সমস্যা সহ নানা শারীরিক জটিলতা। তার চেয়েও বড়ো সমস্যা ক্রমে নিঃস্ব, কপর্দকহীন হয়ে পড়েছেন বনরাজ। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, ব্যাংকের খাতায় এক টাকাও জমা নেই তার। বহুদিন ধরে ভালো করে খাওয়া জোটে না আর। নিজের বলতে দীর্ঘদিনের এক বিশ্বস্ত পরিচারক। অতীতে ঠিক একই রকমভাবে তিলেতিলে সবার অলক্ষ্যে হারিয়ে গেছিলেন আরেক বিস্ময়কর সুরকার অজিত বর্মন। কেউ তার খোঁজও রাখেনি। বলিউডে এই ধরনের ঘটনা নতুন বা অস্বাভাবিক কিছু না। কথায় আছে না—”সেনোরিটা! বড়ে বড়ে দেশো মে অ্যায়সি ছোটি ছোটি বাত হোতি রহতি হ্যায়!”
তবু সৌভাগ্যের বিষয়, ‘মিড ডে’-র সেই প্রতিবেদন পড়ে এগিয়ে এসেছেন বহু মানুষ। এগিয়ে এসেছেন বলিউডের বহু নামজাদারা। দেশ-বিদেশ থেকে ক্রমেই সাড়া দিচ্ছেন, অকৃপণ নিঃস্বার্থ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন বনরাজ ভাটিয়ার অসংখ্য গুণগ্রাহীরা। তাঁকে নিয়ে একটি বিশেষ সাম্মানিক গ্রন্থপ্রকাশের পরিকল্পনাও নেওয়া হচ্ছে। গড়া হচ্ছে ‘ফাণ্ড’। সকলের একটাই উদ্দেশ্য—এইভাবে যেন সবার অলক্ষ্যে বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে না যান সুরকার বনরাজ ভাটিয়া। আবারও যেন তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। সঙ্গীতে ফিরে আসতে পারেন পুনরায়।
সেই একই প্রার্থনা কলমচিরও। এই লেখার মাধ্যমে সেই বিরল সঙ্গীতসাধকের প্রতি অফুরান শুভ কামনা, শ্রদ্ধার্ঘ্য ও তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। আবারও স্বমহিমায় ফিরুন বনরাজ। আবারও যেন শুনতে পারি আমরা পিয়ানোর সামনে বসে তিনি গাইছেন, শ্যাম বেনেগলের ‘সূরজ কা সাতওয়া ঘোড়া’ চলচ্চিত্রে তাঁরই দেওয়া সেই অপার্থিব সুর—
ইয়ে শামে সব কি সব শামে
ক্যয়া ইনকা কোই অর্থ নহি?
ঘবড়াকে তুমহে যব ইয়াদ কিয়া
ক্যয়া উন শামো কা অর্থ নহি?…
।। আমিনা পেরেরা।।
আমিনা আন্টিকে প্রথম দেখি হাওড়া স্টেশনে। আজ থেকে প্রায় সাত-আট বছর আগে। সেবার আমাদের প্রথম মাইহার যাত্রা। আমরা মানে আমি, উদয়, চন্দনাদি (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাটেক বিভাগের অধ্যাপিকা চন্দনা সেনগুপ্ত)। ছিল সিরাজ ও সায়কও। সেবার মাইহার মিউজিক কনফারেন্সে সিরাজ (ধ্যানেশ বাবুর সুযোগ্য পুত্র সিরাজ আলি খান) বাজিয়েছিল। এবং এককথায় তা অসাধারণ। তাদের সঙ্গেও তখনই আলাপ। কিন্তু সবাইকে ছাপিয়ে মধ্যমণি ‘তিনি’। আমাদের মতো নেহাতই অনভিজ্ঞদের তিনিই মাতৃসম পথপ্রদর্শক। আমাদের সবার আমিনা আন্টি।
প্রথম আলাপেই তাকে ‘আন্টি’ বলে ডেকেছিলাম। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, সেই প্রথম আলাপের ঘোর কাটতে চাইছিল না সহজে। ইনিই সেই আমিনা পেরেরা, যার কথা এত শুনেছি! কিংবদন্তি সরোদবাদক উস্তাদ আলি আকবর খাঁ সাহেবের মেয়ে, ‘বাবা’ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের নাতনি, অন্নপূর্ণা দেবী যার পিসি। মাইহার ঘরানার সঙ্গে যার সম্পর্ক পরতে পরতে। আমাদের মতো তুচ্ছ মানুষদের কাছে এই সান্নিধ্য পরম ভাগ্যের বিষয়।
কিন্তু যতই তাকে দেখেছি, অবাক হয়েছি আরও বেশি। বিশ্ববিখ্যাত শাস্ত্রীয় সংগীত ঘরানা ও পরিবারের সদস্যা, অথচ কী মাটির মানুষ। যেন কতদিনের চেনা। কী প্রশান্তি তার মুখে, কী ব্যাপ্তি তার কথায়, কী স্নেহ-মায়া-মমতায় গড়া সেই ব্যক্তিত্ব। সারা রাস্তা এক সঙ্গে গল্প করতে করতে আসা। কত কথা। কত অজানা ইতিহাস। ওনার ছোটোবেলা, দাদু (আলাউদ্দিন খাঁ)-র গল্প, দিদিমা (মদিনা বেগম)-এর গল্প, প্রবাদপ্রতিম পিসি-বাবা-দাদাদের কথা। এবং অবশ্যই মাইহারের গল্প। উনি বলছেন, মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনেছি আমরা। চোখের সামনে যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছিল সমগ্র মাইহারের সাংগীতিক সাম্রাজ্য। সময় কেটেছিল অজান্তে।
মাইহারে নেমে আগে গেছিলাম ‘আশ্রমে’। বাবা উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের স্মৃতিবিজড়িত বাসস্থান-‘মদিনা ভবন’। সেই বাড়ি যেখান থেকে বেরিয়ে এসেছেন রবিশংকর আলি আকবর নিখিল ব্যানার্জি যতীন ভট্টাচার্য পান্নালাল ঘোষ আশিস খাঁ ধ্যানেশ খাঁ-র মতো কিংবদন্তি শিল্পীরা। আজও যেখানে কান পাতলে সেতার-সরোদ-বাঁশির আওয়াজ বাতাসে ভেসে বেড়ায়। আমিনা আন্টি নিজে সব ঘুরিয়ে দেখিয়ে ছিলেন। এমনকি রাতে নিজের হাতে রেঁধে খাইয়েও ছিলেন পরম যত্নে। যত না আয়েশ, তার চেয়ে বেশি বিস্ময় জড়িয়ে প্রতিটি পদে। সেই স্বপ্নের পরিবেশ, সেই বাড়ি, সেই অজস্র স্মৃতি সব যেন মিলেমিশে একাকার। পরে, একে একে সারদা দেবীর আশ্রম, মাইহার কেল্লা, মিউজিক কনফারেন্স সব স্বপ্নের মতো কাটল। আলাপ হল বহু মানুষের সঙ্গে। প্রাণেশ কাকা (বিখ্যাত তবলিয়া প্রাণেশ খাঁ) তাদের অন্যতম। সিরাজের সঙ্গে তার সঙ্গত ভোলার নয়। এর মাঝেই বাবা আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের মাজারে ফুল চড়ানো, প্রার্থনা করা, মাইহার ঘুরে দেখা সব একে একে সুসম্পন্ন। এক সময় একসঙ্গে ফিরেও এলাম কলকাতায়।
এরপরে আমিনা আন্টির সেই রানিকুঠির বাড়ির দরজা অবারিত হয়ে যায় আমাদের কাছে। চন্দনাদি তাঁর বহুদিনের ছাত্রী। তার কাছে এসব পূর্ব-পরিচিত। কিন্তু আমার মতো নভিসের কাছে তা সরস্বতীর আপন দেশ। কতদিন হয়েছে রবিবার-রবিবার ছুটে গেছি সেখানে। আমি তার ছাত্র হতে পারিনি কখনও, কিন্তু তা বলে কখনও কোনও আড়াল টানেননি তিনি। বরং নিজের থেকে দেখিয়ে দিয়েছেন বহু রাগের চলন, সরগম, তান বা মীড়খণ্ডের আসল রূপ। সেতারকে তার হাতে কথা বলতে শুনেছি। বিস্ময়ে কেটে গেছে অগুনতি সময়। না চাইতেও দিয়ে গেছেন অনেক কিছু, অবারিত হাতে।
সম্প্রতি, প্রয়াত হয়েছেন আমিনা আন্টি। বন্ধু সিরাজের ফেসবুক পোস্ট থেকে জানতে পারি এই দুঃসংবাদের কথা। বহু কথা মনে পড়ে যাচ্ছেসেই সূত্রে। এইসব মানুষের কথা কতটাই বা জানি আমরা। প্রচারের আড়ালে থেকে যারা এগিয়ে দিয়েছেন তার ঘরানাকে। সিরাজ, সায়ক, দিশারী বা দেবাঞ্জন এই ঘরের ছেলে। আমার চাইতে অনেক বেশি সান্নিধ্য পেয়েছে তারা এই মহিয়সীর। তারা ভাগ্যবান। আমার সামান্য প্রাপ্তির ঝুলি ঘেঁটে আমিনা আন্টিকে এইটুকু শ্রদ্ধাঞ্জলি। আমিনা আন্টি, যেখানেই থাকুন আমার স্থির বিশ্বাস সেখানে আবার নতুন করে সেতার বেজে উঠবেই…নাম না জানা রাগে।
।। আমার গুরুমা।।
ইদ আসলে আমার চাচির কথা খুব মনে পড়ে।
আমার গুরুমাকে চিরকাল ‘চাচি’ বলে ডেকে এসেছি। জানি না কেন কখনও ‘মা’ বলে ডাকতে পারিনি। অথচ আমার গুরু উস্তাদ মতিউর ইসলম সাহেবকে প্রথম দিন থেকে ‘আব্বা’ বলেই ডেকেছি। ইদ আসলেই এখন খুব চাচির কথা মনে পড়ে। অত্যন্ত বিদূষী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহিলা। খুব গরিব ঘরের মেয়ে। ভালো ছাত্রী ছিলেন। সেই সময়কার বি এ, বি টি। বজবজের কাছে একটি স্কুলে পড়াতেন। মনে আছে, সকাল সকাল নামাজ, স্নান সেরে, রান্নাবান্না করে অপেক্ষা করতেন। সে যে কত রকমের পদ তা গুনে শেষ করা যেত না। আমিও সেই লোভে লাফাতে লাফাতে হাজির হতাম। কাবাব, বিরিয়ানি, সিমাইয়ের পায়েসের গন্ধে ম ম করত ঘর। কিন্তু তা হলে কী হবে, সামনে ঠিক মূর্তিমান বিভীষিকার মতো ‘আব্বা’ দাঁড়িয়ে। কড়া হুকুম হত—”বিরিয়ানি পরে হবে। আগে দেখি নতুন যে ‘পালটা’ শেখালাম সেটা উঠেছে কিনা। আগে রেওয়াজ, পরে কাবাব।” হা হতো’স্মি! ইদেও ছাড় নেই! অগত্যা আব্বার পিছন পিছন ব্যাজার মুখে সরোদ নিয়ে বসে পড়া ও ঝাড়া তিন ঘন্টার ভয়ংকর সিটিং। প্র্যাকটিস করব কী, খাবারের গন্ধে তখন মধ্যপ্রদেশে খণ্ডযুদ্ধ। যতবার পালটা সাধতে যাচ্ছি, তত হচ্ছে ভুল, ততই চড়ছে আব্বার মেজাজ—’শুধু বিরিয়ানি, মণ্ডা-মিঠাই খেলেই হবে। রেওয়াজ কে করবে শুনি। এসব কি বাজনা হচ্ছে? ভুতের কেত্তন?” যখন আর পারা যাচ্ছে না, খিদের চোটে প্রাণপাখী খাঁচাছাড়া হবার জোগাড় তখনই ত্রাতার ভূমিকায় আসরে নামতেন চাচি। খুব ঠান্ডা গলায় বলতেন ”ছেলেটা সকাল থেকে কিছু না খেয়ে বসে আছে। খেয়ে উঠেও তো বাজাতে পারে। মা সরস্বতী রাগ করবেন না। ইদের দিনে কি এতটুকু সহজ হওয়া যায় না?” সামান্য জিজ্ঞাসা আর তাতেই ‘ম্যাজিক’। আব্বা হুকুম করলেন ”যাও, খেয়ে উদ্ধার করো। তোমার চাচির কথার উপর তো কথা নেই।” শুধু বলারই অপেক্ষা। লাফিয়ে উঠে গপাগপ খেতে শুরু করে দিতাম। চাচি আদর করে পরম মাতৃস্নেহে এই পদ, সেই পদ তুলে দিতেন পাতে। মাথায় হাত বুলিয়ে বলতেন—”খা বেটা…ভালো করে খা। আর শোন, মন দিয়ে রেওয়াজ করিস বাবা। পালটা তুলতে পারলে কিমা রেঁধে খাওয়াব। রেওয়াজ করবি তো বল?”
আজ এত বছর হয়ে গেছে ওই স্পর্শ এখনও ভুলিনি। বয়স হয়েছে দুজনেরই, কিন্তু সেই ভালোবাসা আজও অমলিন। বিয়েতে এসেছিলেন। আমার স্ত্রী সুদেষ্ণাকে অনেক আদর, আশীর্বাদ করেছেন। শেষবার কলকাতা গিয়ে দেখা করে এসেছি। কিন্তু আজও ইদের সময় এই মানুষ দুটোর কথা খুব মনে পড়ে। ‘আম্মি’ বলে ডাকতে ইচ্ছা করে খুব সেই মানুষটাকে। ১৫০০ কিমি দূরে সুদূর দিল্লির এই ঘরের এককোণে রাখা সরোদটার দিকে তাকিয়ে খুব চাচির কথা মনে পড়ছে আজ। আমার চাচি, যাকে আমি কখনও ‘মা’ বলে ডাকতে পারিনি।
ইদ মুবারক আব্বা…ইদ মুবারক আম্মি!
।। অমল দত্তের তবলা।।
অমল ‘ডায়মন্ড’ দত্ত চলে গেছেন, বহুদিন হল। সঙ্গে নিয়ে একুশ তোপের সেলামী। ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটা যুগের অবসান। না, আমি তার কিংবদন্তি ফুটবল কোচিং বা ‘ম্যান মার্কিং’ নিয়ে বিশ্বমানের চিন্তা ভাবনা বিষয়ে কোনও ভাবগম্ভীর আলোচনা করতে বসিনি। সে দুঃসাহস বা যোগ্যতা আমার নেই। টিভিতে দত্তবাবুর শেষযাত্রা দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়েছিল যা না বলে পারছি না। খুব কম লোকই জানেন যে অমল দত্ত ভালো ফুটবলার ও কোচের পাশাপাশি কিন্তু অসাধারণ ভালো তবলিয়া ছিলেন। সম্ভবত ওনার বাবার কাছে তালিম পেয়েছিলেন। বিদ্বজ্জনেরা ভালো বলতে পারবেন নিশ্চয় এ বিষয়ে।
বহুবছর আগে, খুব সম্ভব দূরদর্শনে একটা অসাধারণ অনুষ্ঠানের সাক্ষী হয়েছিলাম। যতদূর মনে পড়ে পয়লা বোশেখের একটা অসামান্য প্রোগ্রাম। তাতে বিখ্যাত ফুটবলারদের ত্রয়ী-বাদন। গানে সুকুমার সমাজপতি, তবলায় অমল দত্ত ও তানপুরায় পি কে ব্যানার্জি। সুকুমারবাবু নিজে অত্যন্ত সুগায়ক। তার ছেলে সন্দীপন সমাজপতিও গুণী শাস্ত্রীয় সংগীতশিল্পী। সেদিন খুব সুন্দর কিছু বাংলা রাগাশ্রয়ী গান গেয়েছিলেন সুকুমারবাবু। পি কে-কে দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে উনি এসবে খুব একটা অভ্যস্ত নন। তবু যথাসাধ্য হাসি মুখে তানপুরা ছাড়ছিলেন। আর এক কথায় অনবদ্য ছিলেন অমলবাবু। আহা, এমন যোগ্য সঙ্গত খুব কম শুনেছি। আলতো ঠেকার মাঝে ফারুক্কাবাদ ঘরানার কী সুন্দর সব কাজ, পেশকার, বোলবাট। মুগ্ধ হয়ে শুনেছিলাম সেদিন। সেই বাজনা শুনলে কে বলবে ইনি দেশীয় ফুটবলে বিশ্বমানের সেই ‘ডায়মন্ড’ চক্রব্যূহের স্রষ্টা। আজ সে কথা আরও একবার মনে পড়ে গেল। দুর্ভাগ্য, ‘ইউটিউব’ ও ‘গুগল’ ঘেটে অনেক চেষ্টা করেও সেই রেকর্ডিং উদ্ধার করতে পারলাম না।
‘গানের ওপারে’ আদৌ যদি কিছু থেকে থাকে, তবে এতক্ষণে ফুটবলের পাশাপাশি দেবাসুরগণকে তবলার তালে তাল মিলিয়ে ৪-১-২-১-২ ছন্দে গোল দেওয়া শেখাতে শুরু করেছেন অমল দত্ত। নতুন ‘হীরক’ জয়ন্তী শুরু হল বলে।
।। কৌতুক গীতি।।
ভারতীয় মেইনস্ট্রিম সিনেমায় ‘মুভি মিউজিক’-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অথচ ‘অবহেলিত’ পর্বটি হল ‘কৌতুক গীতি’ বা কমিক বা স্যাটায়ারিকাল কম্পোজিশন। জানি বিষয়টি নিয়ে বহু তর্ক-বিতর্ক উঠবে, তবু আলোচনার স্বার্থে বলা যেতেই পারে যে গল্পের খাতিরে যেমন রোম্যান্টিক, স্যাড সং বা দুঃখের গান, ভক্তিগীতি বা ডিভোশনাল সং, নেচার সং এমনকি ইরোটিক সং-ও বারবার উঠে এসেছে, তেমনই কিন্তু ভারতীয় সিনেমায় নিজের স্বতন্ত্র জায়গা করে নিয়েছে বিভিন্ন ভাষার বিভিন্ন সিনেমায় উঠে আসা ‘কমিক-কম্পোজিশন’ বা কৌতুক গীতির ব্যবহার। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই বিশেষ পর্যায়টির গান নিয়ে লোকজনের মধ্যে তেমন কোনও উৎসাহ বা হেলদোল আজকাল আর চোখে পড়ে না। এ বড়ো দুঃখের। হয়তো দৈনন্দিন জীবন থেকে নির্ভেজাল হাসি-ঠাট্টা-মশকরার রসদ ক্রমে নিম্নমুখী হতে হতে হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের জীবন থেকে…দ্রুত…খুব দ্রুত…
মনে করে দেখুন, কিশোর কুমার-এর ‘হাফ টিকিট’ (১৯৬২) সিনেমার সেই ‘চিল চিলচিল্লাকে কাজরে শুনায়ে’র মতো ‘ননসেন্স ভার্স’ বা ‘জিদ্দি’ (১৯৬৪) সিনেমায় মেহমুদ-এর লিপে মান্না দে-র কন্ঠে দরবারী কানাড়া রাগে ‘প্যার কি আগ মে তন বদন জ্বল গয়া’র কথা। মনে করুন, সুনীল দত্ত ও সায়রা বানুর ‘পড়োসন’ (১৯৬৮) সিনেমায় রাহুল ‘পঞ্চম’ দেব বর্মণ-এর সেই অসাধারণ ‘কাল্ট কম্পোজিশন’ —’এক চতুরনার বড়া হোশিয়ার’-র মতো গান, যাকে অমরত্ব দিয়েছিলেন মান্না দে ও কিশোর কুমার-এর মতো গায়কেরা। বেহাগ, বাগেশ্রী, দেশ ও ছায়ানটের মতো একাধিক রাগের মিশ্রণ (মিশ্ররাগ) ছিল তাতে। বাংলাতেও এমন দৃষ্টান্ত কম নেই। সত্যজিৎ রায়-এর ‘গুগাবাবা’ (১৯৬৯) থেকে ‘হল্লা চলেছে যুদ্ধে’ বা ‘শ্রীমান পৃথ্বীরাজ’ (১৯৭২) সিনেমায় ‘কৃপা করে করো মোরে রায় বাহাদুর’ গানগুলো তালিকার শীর্ষে থাকবে। আজ হঠাৎই এই হাসির গানের প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল এই গানটি—’ম্যয় হু নম্বর এক গবাইয়া’-র মতো অসাধারণ মজাদার অথচ অখ্যাত গানটির কথা।
১৯৯৬ সালে রিলিজ হয় ডেভিড ধাওয়ান-গোবিন্দা জুটির আরও একটি ব্লকবাস্টার ছবি ‘সাজন চলে শ্বশুরাল’। একটা সময় ছিল যখন ডেভিড ধাওয়ান আর গোবিন্দা মানেই সিনেমা সুপারহিট। এ ছবিও তার ব্যতিক্রম নয়। গোবিন্দা একাই একশো, আর তার সাথে তুমুল পাল্লা দিয়ে সতীশ কৌশিক, কাদের খান, শক্তি কাপুর-এর অভিনয়। দর্শকেরা হাসতে হাসতে চেয়ার উলটে লুটোপুটি খেত। শুধু সিনেমাই নয়, ব্যাপক হিট হয়েছিল ‘সাজন চলে’ শ্বশুরাল-এর গানুগলিও। নাদিম-শ্রবনের সুরে, সমীরের লেখায় ছবির গানগুলি রীতিমত লোকেদের মুখে মুখে ফিরত। কিন্তু এত কিছু হওয়া সত্ত্বেও কোথাও যেন হারিয়ে গেছিল ‘ম্যায় হু নম্বর এক গবাইয়া’-র মতো অসম্ভব মজাদার, হাস্যকৌতুকে ভরপুর অথচ কঠিন রাগাশ্রয়ী গানটি। এও এক বিস্ময়!
সিনেমার গল্পে জানা যায়, অনেকটা ‘গুগাবাবা’র আদলে ‘শ্যামসুন্দর’ ওরফে ‘শ্যাম’ (গোবিন্দা)-র কথা, যে তার দক্ষিণী তবলাবাদক বন্ধু ‘মুত্তুস্বামী’ ওরফে ‘মুত্তু’ (সতীশ কৌশিক)-এর সঙ্গে বম্বে এসেছে গায়ক হবে বলে। ঘটনাচক্রে, একটি রেকর্ড কোম্পানির অনুষ্ঠানে তাদের ট্যালেন্টের পরিচয় দিতে গিয়ে মুখোমুখি সংঘাত—গানের লড়াইয়ে নামতে হয় এক জাঁদরেল শাস্ত্রীয় সংগীতের ওস্তাদের (শক্তি কাপুর) বিরুদ্ধে। সৃষ্টি হয় ‘ম্যায় হু নম্বর এক গাওয়াইয়া’। গানটি গেয়েছিলেন নব্বই দশকের অন্যতম বিখ্যাত গায়ক বিনোদ রাঠোর (যিনি ততদিনে ‘আশিকি’, ‘সাজন’ ও ‘দিওয়ানা’তে গেয়ে জনপ্রিয়), নবাগত কুনাল গাঞ্জাওয়ালা ও পণ্ডিত সত্যনারায়ণ মিশ্র। অদ্ভুত মুনশিয়ানায় গানের কথা সাজিয়ে ছিলেন সমীর।
এক কথায় গানটি ছিল সবদিক দিয়ে ব্যতিক্রমী। সেই সময় ওই ধারার সিনেমায় (পপুলার কমেডি) এই রকম কঠিন রাগাশ্রয়ী গানের ব্যবহারের কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। তাও এমনি সেমনি রাগ নয়, একেবারে দরবারী কানাড়ায় বানানো হয়েছিল গানটি। তেমনি মজাদার লিরিক। শুনতে মজার হলেও গানটি ছিল অত্যন্ত কঠিন। বিনোদ রাঠোর নিজে দীর্ঘদিন তাঁর বাবা পণ্ডিত চতুর্ভুজ রাঠোর-এর কাছে শাস্ত্রীয় সংগীতের তালিম নিলেও এ জাতীয় গান আগে কখনও গাননি। সদ্য সদ্য ইন্ডাস্ট্রিতে পা রাখা কুনাল গাঞ্জাওয়ালাকে রাখা হয় সাপোর্টিং ভোকাল হিসেবে। আসল দায়িত্বটি নিয়েছিলেন পণ্ডিত সত্যনারায়ণ মিশ্র। দরবারীর বক্রতান, সরগম বিন্যাস ও সর্বোপরি তারানার অংশটিতে জাঁদরেল ওস্তাদের লিপে অসাধারণ গায়কির পরিচয় রাখেন মিশ্র। অথচ লোকে তাঁকে কবেই ভুলে গেছে। ভুলে গেছে, অমিতাভ বচ্চনের ‘নমকহালাল’ (১৯৮২) সিনেমায় বাপি লাহিড়ির সুরে সেই বিখ্যাত ‘পগ ঘুংরু বাঁধ মীরা নাচিথি’ গানে কিশোর কুমার-এর পাশাপাশি তার গানের কথা। সেই গানে একটি বেশ শক্ত ‘তানকর্তব’ ছিল যা তিনিই গেয়েছিলেন। লোকে কিশোর কুমারকে মনে রাখলেও ভুলে গেছে সত্যনারায়ণ মিশ্র নামের এই অসম্ভব প্রতিভাবান শাস্ত্রীয় সংগীত শিল্পীটির কথা, যার কাজই ছিল শক্ত শক্ত রাগাশ্রয়ী গানে ‘সাপোর্টিং ভোকাল’ রূপে কাজ করা। বছর আট-নয় আগে নিতান্তই অবহেলায়, অনাদরে মারা যান সত্যনারায়ণ মিশ্র।
কিন্তু এত কিছু বাঁধা কাটিয়েও শেষপর্যন্ত সার্থকতা পায় ‘ম্যায় হুঁ নম্বর ওয়ান’ গানটি। সিনে ইন্ডাস্ট্রিতে প্রবল প্রশংসিত হন সেই সময় গানটির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা প্রত্যেক কলাকুশলী। সমস্ত কাগজে গানটি নিয়ে উঠে আসে একাধিক ‘পজেটিভ রিভিউ’। পায় সেরা গানের জন্য ফিল্মফেয়ার এওয়ার্ডের নমিনেশন। প্রশংসিত হন রাঠোর ও মিশ্র, দরবারী কানাড়ার এমন স্বতন্ত্র ও ব্যতিক্রমী গায়নের জন্য। তবে তা অল্প কিছুদিনের জন্যই। তারপরেই বিস্মৃতির আড়ালে কোথায় যেন হারিয়ে যায় গানটি। আরও হাজার হাজার গানের মতোই
সাধারণ দর্শককে হাসিতে ভরিয়ে তুললেও গানটি সে অর্থে কখনও যোগ্য স্বীকৃতি পায়নি। মানুষও একসময় ধীরে ধীরে ভুলে যায় বলিউডের অন্যতম সেরা এই ‘কমিক কম্পোজিশন’টিকে, যা আদতে হয় দরবারী কানাড়ার দুর্লঙ্ঘ, দুরুহ ভিতের উপর তৈরি। আজও যা বিস্ময়কর মুগ্ধতায় ভরপুর।