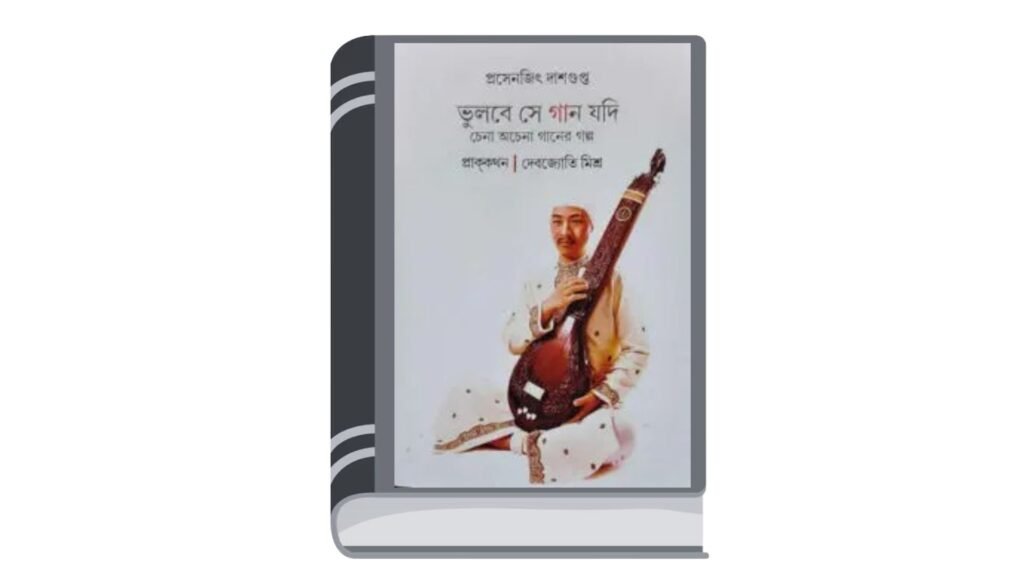ভুলবে সে গান যদি – ২০
।। ইউফনি।।
কোনও একটি সিনেমা দেখার পর মোটামুটি দু’রকম প্রতিক্রিয়া উঠে আসে। এক, ভালো লাগা এবং অবশ্যই ভালো না লাগা। কিন্তু বহু ‘ভালো না লাগা’ সিনেমার মধ্যেও এমন কিছু বিশেষ পর্ব থাকে, যা আমাদের গভীরভাবে স্পর্শ করে। অমিতাভ বচ্চন-অনিল কাপুরের ‘আরমান’ (২০০৩) সেই রকমই একটি সিনেমা। ‘আরমান’ যখন রিলিজি করেছিল তখন আমার মাস্টার্স শেষ হওয়ার পথে। চিকিৎসক পিতা পুত্রের আদর্শ, তাদের স্বপ্ন, প্রতিকূলতা, ভালোবাসা ও উত্তীর্ণ হওয়ার গল্প শুনিয়েছিল ‘আরমান’। সেই অর্থে এর গল্প বা ‘সিনেম্যাটিক ট্রিটমেন্ট’ তেমন ভালো না লাগলেও পিতা-পুত্রের অদ্ভুত কেমিস্ট্রি কিন্তু মন্দ লাগেনি। আর অদ্ভুতভাবে টেনেছিল ‘ইউফনি’। সিনেমাটির মিউজিকের দায়িত্বে ছিলেন শঙ্কর-এহসান-লয়, ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরে রাজু সিং। জাভেদ আখতার-এর কথায় সিনেমার গানগুলি হিট হয়েছিল। তবে গভীরভাবে ছুঁয়ে গেছিল ‘ইউফনি’ অংশটি।
কাজ থেকে ফেরা ক্লান্ত, বিধ্বস্ত ছেলেকে বাবা পরামর্শ দিচ্ছেন সংগীতের নিভৃত, শান্তির আশ্রয়ে বসতে। বলছেন, এই সেই আশ্রয় যা সারাদিনের সব ক্লেদ, দুঃখ, মনস্তাপ ভুলিয়ে দিতে সক্ষম। পথ দেখাতে সেই পিতা নিজের হাতে তুলে নেন বেহালা, ছেলের ঠোঁট স্যাক্সোফোন। তারপর উঠে আসে মিনিট তিনেকের এক অসাধারণ যুগলবন্দী। রাগ ইমনে কর্ণাটকী ভায়োলিন আর স্যাক্সোফোনে এমন অসাধারণ ও ব্যতিক্রমী দ্বৈত-বাদন খুব কম শোনা যায়। এর প্রত্যেকটি স্ট্রোক, নোট, মীড়খণ্ড ও পুকার এতটাই নিখুঁত যে বহুদিন তার রেশ রয়ে যায় মনে। যিনি ‘স্যাক্স’ বাজিয়েছেন তার তুলনা নেই। বেহালাবাদকের জন্য যে কোনও প্রশংসাই কম মনে হয়। বহুবার চেষ্টা করেছি, এই অনবদ্য বাদনের নেপথ্যে কারা রয়েছেন তা জানার…দুর্ভাগ্য, সমায়াভাবে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কিন্তু আজও, এতদিন পরেও এই অসাধারণ কম্পোজিশন মনে গেঁথে রয়েছে। দুই সেরা অভিনেতা তাদের মতো করে যথাসাধ্য ঢেলে দিয়েছেন দৃশ্যটিকে সার্থকতা দিতে।
‘ইউফনি’র অর্থ শ্রুতিমাধুর্য। কিন্তু আমার কাছে তা আরও বেশি কিছু। যতবার এই ছোট্ট পিসটি শুনি, আমার নিজের ছেলের কথা মনে পড়ে। জুনে সে দু’বছরে পা দেবে। আমার থেকে অনেকটা দূরে, তার মায়ের পাশে এখন সে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। আর আমি রাত জেগে জেগে সেই দিনটার জন্য অপেক্ষা করে থাকি, যেদিন দিনের শেষে ঘরে ফিরে বাপ-ব্যাটাতে একসাথে রেওয়াজে বসবো। যুগলবন্দীতে হবে সমানে সমানে লড়াই। তারপর, ইচ্ছে করে ভুল করব, সরগমে, বেসুরো হব আর হাসতে হাসতে আমার ছোটোখাটো ভুলচুকগুলো ধরিয়ে দেবে সে। ছেলের সেই হাসিতে আমিও মেলাবো তাল…সুর…লয়!
এর চেয়ে ভালো ‘ইউফনি’ আর কি হতে পারে…তাই না! সেই দিনটার অপেক্ষায় আমি রাত জেগে স্বপ্ন দেখতে থাকি। আজও…ভীষণভাবে!
।। দ্য ওয়াটার।।
১৯৫৫ সাল।
সত্যজিৎ রায়-এর কালজয়ী ‘পথের পাঁচালী’র পথচলা শুরু। সংগীত পরিচালনায় রবিশঙ্কর (১৯২০-২০১২)। তখনও তিনি ‘পণ্ডিত রবিশঙ্কর’ হয়ে উঠেছেন কিনা সন্দেহ। কারণ ওপেনিং ক্রেডিট ছিল ‘পণ্ডিত’ বর্জিত। কিন্তু রবিশংকর, রবিশংকরই। তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম। চলচ্চিত্রের পাশাপাশি ‘মাইলস্টোন’ গড়েছিল ছবিটির সংগীতও। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে রচিত রবিশংকর-এর সুরে ‘পথের পাঁচালী’র কালজয়ী থিম মন্ত্রমুগ্ধ করেছিল তামাম সিনেমা-প্রেমীদের। আজও সে মুগ্ধতা অটুট।
রবিশঙ্করের সেতার ও অলোকনাথ দে-এর বাঁশি—এই দুইয়ের সঙ্গমে, সুর-উচ্ছ্বাসে সেই অপার্থিব আবহের সৃষ্টি। যার সুরের মায়াজাল অমরত্ব দিয়েছিল বিভূতিভূষণের নিশ্চিন্দিপুরকে। সেই সুরবিন্যাসে প্রাণ পেয়েছিল ‘হরিহর’, ‘সর্বজয়া’, ‘অপু’, ‘দুর্গা’ ও ‘ইন্দিরা ঠাকরুন’-এর মতো চরিত্রগুলি।
বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতিহাসে ‘পথের পাঁচালী’র জন্য অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবহ সংগীতের শিরোপা আজও তাই রবিবাবুর দখলে।
১৯৯৭ সাল।
মুক্তি পেল ‘টাইটানিক’। জেমস ক্যামেরন-এর ম্যাগনাম ওপাস। ‘পথের পাঁচালী’র মুক্তির পাক্কা ৪২ বছর পরে। ডুবন্ত জাহাজে ভয়, আতঙ্ক, মৃত্যুমিছিল ছাপিয়ে উঠে এল ভালোবাসা, বন্ধুত্ব ও নির্ভরতার জয়গান। ‘রোজ বিউটেকার’ (কেট উইন্সলেট) আর ‘জ্যাক ডসন’ (লিওনার্দো ডি ক্যাপ্রিও)-এর ভুবনজয়ী প্রেম-আখ্যানে আপ্লুত হয়েছিল গোটা পৃথিবী।
চিত্রনাট্য, অভিনয় ও পরিচালনার পাশাপাশি সংগীতেও চরম উৎকর্ষের নজির রেখেছিল ‘টাইটানিক’। ছবির সংগীত পরিচালনার জন্য প্রশংসা কুড়িয়ে ছিলেন জেমস ‘রয়’ হর্ণর (১৯৫৩-২০১৫)। তার সুরে বিখ্যাত গায়িকা স্যিলিন ডিওন-এর ‘মাই হার্ট উইল গো অন’ অসম্ভব জনপ্রিয়তা পায়।
গানের পাশাপাশি ‘টাইটানিক’-এর ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরে মোহিত হয়েছিলেন সংগীত প্রিয় মানুষেরা। ‘ওশন অফ মেমোরিজ’, ‘টেক আর টু দ্য সি, মি. মার্ডক’, ‘দ্য সিনকিং’, ‘ডেথ অফ টাইটানিক’, ‘হাইম অফ দ্য সি’র মতো ট্র্যাকগুলি আজও অবিস্মরণীয়।
সে বছর ১১টি অস্কার জিতে ইতিহাস গড়েছিল জেমস ক্যামেরন-এর ‘টাইটানিক’। তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালনা ও ‘অরিজিনাল সং’ ক্যাটাগরিতে দুটি অস্কার ছিনিয়ে নেন জেমস হর্ণর।
২০০৫ সাল।
মুক্তি পাওয়ার আগে থেকেই বিতর্ক উস্কে দিয়েছিল দীপা মেহতা-র ‘ওয়াটার’। দীপার ‘এলিমেন্টস ট্রিলজি’ (তার আগে তুমুল বিতর্কের ঢেউ তুলেছিল ‘ফায়ার’ ও ‘আর্থ’-র শেষ পর্ব।
ব্রিটিশ জমানায় ভারতে বিধবাদের করুণ অবস্থা, ব্রাহ্মণ্যবাদের আস্ফালন ও সমাজ থেকে একঘরে হওয়া অসহায় মহিলাদের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের এক নয়া দিগদর্শন তুলে এনেছিলেন দীপা।
কিন্তু এত সহজসাধ্য ছিল না সেই কাজ। কট্টরপন্থী হিন্দুসমাজের রোষের আগুনে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল শুটিং। দেশ ছেড়ে শ্রীলঙ্কা গিয়ে শুটিং শেষ করেন দীপা। পরবর্তীকালে ইতিহাস গড়েছিল লিজা রে, সীমা বিশ্বাস, জন আব্রাহাম অভিনীত ‘ওয়াটার’।
সিনেমার পাশাপাশি প্রবল সমাদৃত, প্রশংসিত হয় ‘ওয়াটার’-এর মিউজিক। এ আর রহমান ও মাইকেল ডানা-র যৌথ সংগীত পরিচালনায় অভূতপূর্ব সাড়া পায় ‘ওয়াটার’। হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সংগীতের সঙ্গে পাশ্চাত্য সংগীতের সেই অপার্থিব মেলবন্ধনে যে সুরের জাদু দেখা দিয়েছিল ‘ওয়াটার’-এ, শ্রুতি মাধুর্যে আজও তা অনবদ্য, চিরকালীন।
‘পথের পাঁচালী’, ‘টাইটানিক’ ও ‘ওয়াটার’। মাঝে কেটে গেছে পাঁচটি দশক। কিন্তু ‘ওয়াটার’-এর সূত্র ধরে ৫০ বছরের ইতিহাস এক লহমায় এসে মিশে গেল সিনে-সংগীতের পরতে, পরতে।
‘ওয়াটার’-এর ব্যাকগ্রাউণ্ড স্কোরের দায়িত্ব সামলেছিলেন কানাডিয়ান সংগীত পরিচালক মাইকেল ডানা। পরে যিনি ‘লাইফ অফ পাই’-র সংগীত পরিচালনার মাধ্যমে প্রভূত প্রশংসা কুড়িয়েছেন, এমনকি অস্কারও পেয়েছিলেন।
মজার বিষয়, ‘ওয়াটার’-এর থিম ও ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরে ডানা অব্যর্থ দক্ষতায় মিশিয়ে দেন ‘পথের পাঁচালী’ ও ‘টাইটানিক’-কে। বিশ্বের প্রথমসারির দুই কম্পোজারের দুটি ভিন্ন রচনাকে এভাবে মিশিয়ে দেওয়ার নজির খুব একটা চোখে পড়ে না। যার ফলে ‘ওয়াটার’-এর কম্পোজিশন শুনতে গিয়ে বারবার উঠে আসবে ‘পথের পাঁচালী’-র ধুন এবং ‘টাইটানিক’-এর কেল্টিক সিম্ফনি।
‘ওয়াটার’-এর মিউজিক নিয়ে তাই আজও রয়েছে বিতর্ক। ‘কম্পোজিশনগুলি কি নেহাতই অনুপ্রেরণা, নাকি সুর-চুরির দৃষ্টান্ত—এই নিয়ে আজও মতভেদ আছে। কিন্তু এ আর রহমান বা মাইকেল ডানা কেউই এ বিষয়ে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করেননি। ‘হাউজ অফ উইডো’-এর মতো বিখ্যাত সেই কম্পোজিশনগুলি তাই আজও রহস্যাবৃত।
দিনের শেষে একটি পর্যায়ে পৌঁছাতেই হয়। তা অনুপ্রেরণা হোক বা ‘সুরচুরি’—’ওয়াটার’-এর থিম-সংগীত যে আসলে সর্বকালের দুই মহান শিল্পী—পণ্ডিত রবিশঙ্কর ও জেমস রয় হর্ণর-এর প্রতি অলিখিত এক অবিসংবাদী সুরের শ্রদ্ধার্ঘ্য, তা নিয়ে সন্দেহ নেই।
।। বড়োদিনের গান।।
অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ ছিলেন জেমস। জেমস লর্ড পিয়েরপঁ। ছোটোবেলা থেকেই বাউণ্ডুলে, উড়নচন্ডী স্বভাবের মানুষ। জন্মেছিলেন ১৮২২ সালে ২৫ এপ্রিল বস্টন, ম্যাসাচুসেটস-এ। বাবা রেভারেন্ড জন পিয়েরপঁ ছিলেন ধার্মিক মানুষ, বস্টনের ইউনিটেরিয়ান চার্চের পাদরি।
দামাল জেমস-এর ছোটোবেলা থেকেই ছিল প্রবল লেখালেখির শখ। ভালোবাসতেন গান-বাজনাও। গান লেখা, সুর দেওয়া শখ ছিল তার। সুযোগ পেলেই স্টাডি রুমের এক কোণে মুখ গুঁজে তাকে লেখালেখি করতে দেখা যেত। মাত্র দশ বছর বয়সে তাকে পড়াশোনার জন্য নিউ হ্যাম্পশায়ারে বোর্ডিং স্কুলে পাঠানো হয়। বোর্ডিং স্কুলে থাকার সময় শীতকালে ঘোড়ায় টানা স্লেজ গাড়ির রেস দেখে রোমাঞ্চিত হয়েছিলেন জেমস। মা মেরি শেল্ডনকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন সেই কথা। কিন্তু রক্তে থাকা উদ্দামতা তাকে তিষ্ঠোতে দেয়নি বোর্ডিং স্কুলে। চার বছরের মাথায় সব শিকেয় তুলে ভেসে পড়েন প্রশান্ত মহাসাগরে, ‘দ্য শার্ক’ নামের একটি তিমি শিকারী জাহাজের নাবিক হয়ে। সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এরপর ২১ বছর পর্যন্ত ইউ এস নেভিতেও কাজ করেন জেমস। যেভাবে আচমকা সব কিছু ছেড়েছুড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছিলেন, তেমনই একদিন ১৮৪৫ সালে তিনি ফিরেও আসেন তার পরিবারের কাছে। মা-বাবার চাপে পড়ে মিলিসেন্ট কউয়ি নামের এক সুন্দরী যুবতীকে বিয়ে করে তিন বাচ্চার বাপ হয়ে ঘোরতর সংসারীও হন।
জেমস পিয়েরপঁ-র গল্প কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ১৮শ শতকের মাঝমাঝি গোটা আমেরিকা জুড়ে ‘গোল্ড রাশে’র যে ধূম জাগে, তাতে শামিল হন জেমসও। সেই উন্মাদনা এমনই মাথায় চাগাড় দেয়, যে ১৮৪৯-এ বউ-বাচ্চা পরিবার সব ফেলে ব্যবসা করতে সানফ্রান্সিসকো পাড়ি দেন তিনি। ফটোগ্রাফার হিসেবে শুরু করেন কাজ। কিন্তু বিধি বাম! এক রাতে বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডের জেরে দেউলিয়া হন জেমস। এত কিছু দুর্যোগের মধ্যেও লেখালেখি ছাড়েননি তিনি। ১৮৫০ সালে রচনা করেন ‘ওয়ান হর্স ওপেন স্লেজ’ ও ১৮৫২ সালে প্রকাশিত হয় ‘দ্য রিটার্ন্ড ক্যালিফোর্নিয়ান’। ১৮৫৬ সালে মারা যান তার স্ত্রী মিলিসেন্ট। জেমস তখন গরিব, কপর্দকশূন্য। পেট চালাতে ও বাচ্চাদের সামলাতে ইউনিটেরিয়ান চার্চের ক্যয়ারে সংগীত পরিচালক ও অর্গানবাদক রূপে যোগ দেন তিনি।
এরপর আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। ১৮৫৭ সালে। একদিকে গোটা ভারতীয় উপমহাদেশে তখন ছড়িয়ে পড়েছে মহাবিদ্রোহের আগুন। ওই বছরই অগস্ট মাসে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন জেমস। এবার সাভানার মেয়র থমাস পার্স-এর মেয়ে এলিজা জেন পার্স হলেন পাত্রী। আর একমাসের মধ্যে সাত বছরের পুরোনো রচনা ‘ওয়ান হর্স ওপেন স্লেজ’ থেকে বেরিয়ে আসে একটি ছোট্ট গান যা একসময় ম্যাসাচুসেটসের মেডফোর্ডে ‘দ্য সিম্পসন ট্যাভার্ন’-এ বসে লিখেছিলেন জেমস, পরবর্তীকালে তা ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্ব জুড়ে। হ্যাঁ, এই গানটিই হল ‘জিঙ্গল বেল!’ আজও ক্রিসমাস বা বড়োদিন এই গানটি ছাড়া সম্পূর্ণ নয়। অথচ একটা সময় ছিল যখন এই গানটির কথা ভুলেই গেছিলেন জেমস লর্ড পিয়েরপঁ। গানটি কিন্তু প্রথমে মোটেই সমাদর পায়নি। ১৯৮৩ সালে যখন ফ্লোরিডাতে দীর্ঘ রোগভোগের পর ৭১ বছর বয়সে মারা যান জেমস লর্ড পিয়েরপঁ, তখনও কেউ চেনে না এই গানটি। ক্রিসমাস পালনের জন্য লেখাও হয়নি গানটি। অথচ শেষ পর্যন্ত ক্রিসমাসের সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গীভাবে জুড়ে যায় বিশ্ববন্দিত সেই গান। বাকিটা ইতিহাস।
বড়োদিন এলে অনিবার্যভাবে গাওয়া হয় ‘জিঙ্গল বেল’, অথচ এই কালজয়ী গানটির স্রষ্টা তথা সুরকারকে কেউ মনে রাখেনি। সময়ের স্রোতে মিলিয়ে গেছেন জেমস লর্ড পিয়েরপঁ।
।। দ্য ক্যাট কনসার্টো।।
‘টম এন্ড জেরি’-কে চেনে না বা ভালোবাসে না, এমন মানুষ পাওয়া দুষ্কর। ১৯৪০ সাল থেকে তারা দুজন আমাদের হাসিকান্না, ভালোবাসা-মনখারাপের সঙ্গী। ইঁদুর-বেড়ালের এমনই মজার কেমিস্ট্রি, যা কিনা সারাবিশ্বের আট থেকে আশি, আবালবৃদ্ধবনিতার মন জয় করেছিল। চল্লিশের দশক থেকে শুরু, উইলিয়াম হানা ও জোসেফ বারবারা-র সেই অমর সৃষ্টি আজও অদ্বিতীয়, অপ্রতিরোধ্য। এম জিএম (মেট্রো গোল্ডউইন মেয়ার)-এর ফ্রেড কুইম্বির ব্যানারে ১১৪টি ‘শটস’ (পরবর্তীকালে অন্যান্য নির্মাতাদের হাত ধরে প্রায় ১৬০টিরও বেশি)-এর দৌলতে ‘টম এন্ড জেরি’-র ঝুলিতে উঠে এসেছিল ৭টি অস্কার যা চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছিল ডিজনিকেও।
১৯৪০-৫৮ সাল পর্যন্ত সয়মকালকে, নিঃসন্দেহে এই সিরিজটির ‘স্বর্ণযুগ’ বলা চলে। এই সময়ের মধ্যে নির্মিত ‘শর্টস’গুলি সবচেয়ে বেশি সাফল্য পায়, পায় জনপ্রিয়তা, কুড়োয় সমালোচনাও। তবু ‘টম এন্ড জেরি’ তার প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি। এই সিরিজে এনিমেশনের পরেই যা সবচেয়ে বেশি শিরোনামে উঠে এসেছিল, তা হল সঙ্গীত পরিচালনা ও নেপথ্য সংগীত। গোটা সিরিজ-টি ‘নির্বাক’ হওয়ায় সংগীতই ছিল ‘টম’ আর ‘জেরি’র নিজস্ব ভাষা। চিন্তা করার বিষয়, এই সিরিজ’টির নির্মাতা, নির্দেশক, কলাকুশলীদের কথা সাধারণ মানুষ জানলেও, ‘টম এন্ড জেরি’র সুরকার স্কট ব্র্যাডলির কথা তারা কেউ জানে না। জানেন না, তার অসামান্য সুর-রচনার কথা, যা শুধু অস্কার জিতেই ক্ষান্ত হয়নি। ক্ষান্ত হয়েছে কালোত্তীর্ণ হয়ে।
সংগীত নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এই সিরিজে। ‘টম এণ্ড জেরি’র মিউজিক যেমন বহু প্রশংসা কুড়িয়েছে, তেমনি আছড়ে পড়েছে নানা বিতর্কেও। আর এসবের কৃতিত্ব মার্কিন কম্পোজার ওয়াল্টার স্কট ব্র্যাডলি (১৮৯১-১৯৭৭)-র। এ পর্যন্ত মোট ১১৩টি এপিসোড মিউজিক দিয়েছেন তিনি। পাশ্চাত্য সংগীতে সিদ্ধহস্ত ব্র্যাডলি প্রথম জীবনে থিয়েটার অর্কেস্ট্রায় পিয়ানো বাজাতেন। পরবর্তীকালে এম জি এম-এর সঙ্গে সংযুক্ত হন। কম্পোজ করেন ‘টম এণ্ড জেরি’র ‘সিগনেচার টিউন’ থেকে শুরু করে তার ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর। ইতিহাস সৃষ্টির পথে হেঁটে গেছিল ‘টম এন্ড জেরি’। রম্য-সংগীত বা ‘funny score’ তৈরিতে তার বিকল্প আর কেউই ছিল না সে সময়ে। বহু বিখ্যাত পাশ্চাত্য সংগীতকার যথা প্যাগানিনি, স্ত্রাভিন্সকি, হিন্ডেমিথ-এর রচনাকে হাস্যকৌতুক পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে এক অন্য ধারার সংগীত রচনা করেন তিনি। নিজেই হয়ে উঠেছিলেন স্বতন্ত্র ঘরানা। অবশ্য সুখের দিন বেশি ছিল না ব্র্যাডলির। ১৯৫৪ সালে এম জি এম-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয় তার। ১৯৫৭ সালে এম জি এম-এর কার্টুন বিভাগটি বন্ধ হয়ে যায়। ‘টম এন্ড জেরি’ হস্তান্তরিত হয় অন্য একটি সংস্থা, ‘রেমব্রান্ট ফিল্মস-এর কাছে। সংশ্লিষ্ট সিরিজের হাল ধরেন স্টিফেন কনিচেক, ডেন এইচ ইলিয়ট, কার্ল ব্রান্ট বা এডওয়ার্ড প্লাম্ব-এর মতো স্কট ব্র্যাডলির উত্তরসুরীরা। যদিও ব্র্যাডলির মতো সেই প্রভাববিস্তার করতে পারেননি কেউই। এরপর আর বেশিদিন কাজ টানতে পারেননি ব্র্যাডলি। ২০ বছর পর ক্যালিফোর্নিয়ার চ্যাটাসওয়ার্থে ৮৬ বছর বয়সে প্রয়াত হন তিনি।
‘টম এন্ড জেরি’র ১১৩টি ‘শর্টস-এ সংগীত দিলেও ওয়াল্টার স্কট ব্র্যাডলি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন ‘দ্য ক্যাট কনসার্টো’তে। ১৯৪৭ সালে ২৬ এপ্রিল মুক্তি পায় ‘ক্যাট কনসার্টো। সাড়ে সাত মিনিটের সেই ‘শর্টস’ আজও এনিমেশনের বিশ্বে এক উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে পরিচিত। এই এনিমেশনে টম-কে দেখা যায় পিয়ানো বাজিয়ের চরিত্রে যার বাজনায় বাগড়া দেয় ছোট্ট ইঁদুর জেরি। পিয়ানো তথা বিখ্যাত ওয়েস্টার্ন ক্লাসিকসের নোটেশনকে (এই ক্ষেত্রে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে রোম্যান্টিক যুগের বিখ্যাত পিয়ানিস্ট ফ্রাঞ্চ লিজ-এর বহুচর্চিত ‘হাঙ্গেরিয়ান রাপ্সডি নম্বর ২’) কীভাবে মজাদার করে তোলা যেতে পারে তা অদ্ভুত মুনশিয়ানায় দেখিয়েছিলেন ব্র্যাডলি। ‘কনসার্টো’ সে বছর সেরা এনিমেশনের অস্কার ছিনিয়ে নিয়েছিল।
তবে এই এপিসোড নিয়ে বিতর্কও ছড়িয়েছিল যথেষ্ট। গল্প চুরির অভিযোগ এনেছিল ‘দ্য ওয়ার্নার ব্রাদার্স’ কোম্পানি। কারণ ওই একই বছর ফ্রিজ ফ্রিল্যাং-এর পরিচালনায় তাদের একটি প্রোডাকশনস ‘বাগস বানি’ খরগোশকে নিয়ে ‘র্যাপ্সডি র্যাবিট’ মঞ্চস্থ হয়। আশ্চর্যের বিষয়, টমের মতো সেখানে ‘বাগস বানি’কেও দেখা যায় পিয়ানো বাজাতে ও আরও কাকতালীয় ভাবে তা ফ্রাঞ্জ লিজ-এর ‘হাঙ্গেরিয়ান রাপ্সডি নম্বর ২’। দুটি ভিন্ন সংস্থা এবং ভিন্ন কার্টুন হওয়া সত্ত্বেও কম্পোজিশন কি করে এতটা মিল? বলাবাহুল্য একে অন্যের বিরুদ্ধে সুর ও প্লট চুরির অভিযোগ এনেছিল দুটি সংস্থা। আকাদেমির টেবিলেও জমা পড়েছিল দুটি পৃথক আবেদন। যদিও শেষ পর্যন্ত বাজি মারে ‘ক্যাট কনসার্টো’, কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই রহস্য, রহস্যই থেকে গেছে।
আজ ‘দ্য ক্যাট কনসার্টো’র মুক্তির প্রায় ৭৩ বছর অতিক্রান্ত। এমনকি ৪২ বছর হল পরলোকে পাড়ি দিয়েছেন ‘টম এন্ড জেরি’র অপ্রতিদ্বন্দ্বী সুরকার ওয়াল্টার স্কট ব্র্যাডলি। তবু আজও, ইতিহাসের পাতাটি সমানে সমানেই ভাগ করে নিয়েছে তারা। একে অন্যের ভাবনাচিন্তা বিকল্পধারার অপরিহার্য পরিপূরক হয়ে।
।। সত্যজিতের অজানা সুরে।।
সেই কবে দেখেছিলাম উৎপলেন্দুবাবুর এই ডকুমেন্টারিটা, ‘দ্য মিউজিক অফ সত্যজিৎ রায়’। আজও মন ছুঁয়ে যায়।
আজও ঘুমের গভীরে শুনতে পাই চেলো বাজছে, বাজছে সেতার, ভায়োলিন, ড্রামস। মোটা ফ্রেমের চশমা চোখে, দীর্ঘদেহী সেই মানুষটি—মুখে পাইপ, একহাতে নোটেশন শিট, অন্যহাত শূন্যে তুলে ‘ঘরেবাইরে’-র থিম রচনা করছেন। সুর করে গাইছেন—’ডা ডাডাডা ডাডা’। আর নেপথ্যে কোরাসে ‘বন্দেমাতরম! বন্দেমাতরম!’ গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে আজও।
এরপরেই দ্রুত বদলে যাচ্ছে দৃশ্য। জ্বলন্ত মশাল ভেদ করে উঠে আসছে সেই পাহাড়ি রাস্তা, কুয়াশা ভেদ করে ঠিকরে পড়ছে নরম আলো, খাদের ধারে দাঁড়িয়ে একলা রায়বাহাদুর ও চকলেট লেগে থাকা মুখে সেই বাচ্চা গোর্খা ছেলেটি, যার অদ্ভুত পাহাড়ি সুরে কুয়াশার চাদর কেটে একটু একটু করে উঠে আসছে ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’। পিছুপিছু ‘গুগাবাবা’, ‘মহানগর’, ‘শাখাপ্রশাখা’, ‘আগন্তুক’—অজস্র সুরের মিছিল!
সত্যজিতের সিনেমা-সংগীতকে ব্যাখ্যা করা এক অসম্ভব স্বপ্নের মতো। কিছুটা হলেও উৎপলেন্দুবাবুর তথ্যচিত্রের পরতে পরতে রয়েছে তার স্বাক্ষর।
সিনেমার থেকে গান বা নেপথ্যে সংগীত বরাবরই বেশি টানে আমায়। সত্যজিতের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। ‘সোনার কেল্লা’-র প্রতি প্রেম ও আকর্ষণ আজ থেকে নয়, সেই ছোটোবেলা থেকে। ততধিক, আকর্ষণ সেই ছবির লোকসংগীত নিয়েও। ফেলুদার থিম ক্রমেই একটা মিথে পরিণত। কিন্তু ‘সোনার কেল্লা’য় ব্যবহৃত মীরার ‘মন মেরা রামরাম রচে’—এই ভজনটি আজও তাঁর স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। কী অসাধারণই না গানটি গেয়েছিলেন মোহিনী দেবী। কী অদ্ভুত সেই সুর।
আর ভিড় ঠেলে ছোট্ট মুকুলের একজোড়া সেই নিষ্পাপ চোখ, ঘুমোতে দেয়নি বহুদিন। মোহিনী দেবীকে এরপর আর তেমন কোনও সিনেমায় গাইতে শুনিনি। কিন্তু এই একটি গানেই তিনি অমর হয়ে রয়েছেন মানিকবাবুর সৃষ্টির পাশাপাশি।
ঠিক যেমনটি, লোকশিল্পী রামজন আম্মুর গাওয়া রাতের পোখরান স্টেশনের সেই ‘ঘুমারে ঘুমা’ রাজস্থানী ফোক বা ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’-এ মালকোষ রাগে গাওয়া রেবা মুহুরির ‘মোহে লাগি লগন গুরু চরণন কী’ মীরা ভজনটি।
।। ‘সারাংশ’ ও অজিত বর্মণ।।
আমাদের দৈনন্দিন জীবনে গানের প্রভাব যে কতটা, তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রতি মুহূর্তে, পল-অনুপলে মিশে আছে যে সুর, তা আমাদের চলার পথের সঙ্গী, পাথেয়। হাজার হাজার সুর, হাজার হাজার ধ্বনি-শব্দ-কথা ঘিরে আছে আমাদের। কিছু গান রয়ে যায় সঙ্গে, সারাজীবন। কিছু হারিয়ে যায় কালের গর্ভে। সংগীতও সিনেমার তেমনই একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সিনেমা তার ১০০ বছরেরও বেশি সুদীর্ঘায়িত ইতিহাসে এমন অনেক গান-সুর-কথা উপহার দিয়েছে যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম আমরা বয়ে নিয়ে চলেছি। এর শুরু আছে, শেষ নেই কোনও। কিন্তু সময়ের এমনই অদ্ভুত এই চড়াই-উতরাই, যার অজানা-অচেনা বাঁকে হারিয়েছে বহু গান, ভেসে গেছে বহু সুর, কথা ও তাদের স্রষ্টারা। এমনই কিছু গান, কিছু অপ্রচলিত, অশ্রুত অধ্যায় নিয়েই পথ চলা। যেমন পরিচালক মহেশ ভাট-এর কালজয়ী চলচ্চিত্র ‘সারাংশ’-এর সংগীত।
১৯৮৪ সালে মহেশ ভাট-এর এই সিনেমার মাধ্যমে যখন বলিউডে ডেবিউ করেন অনুপম খের, কেউ ভাবতেও পারেননি পরবর্তীকালে তা ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে মাইলফলকে পরিণত হবে। মৃত ছেলের অস্থিকলস নিয়ে এক রিটায়ার্ড স্কুল টিচার (অনুপম খের) ও তার শোকার্ত স্ত্রী (রোহিনী হাত্তাঙ্গদী)-র আপসহীন লড়াই, একাকিত্ব আর অসহায়তার ঘন অন্ধকারে একটু একটু করে তলিয়ে যাওয়ার আগে আবারও বেঁচে থাকার দাবিতে জীবনের পথে পথ-হাঁটার গল্প কেউই কখনও ভুলবে না। তিন তিনটি ফিল্মফেয়ার এওয়ার্ড ও ১৯৮৫ সালে একাডেমির মঞ্চে বিদেশি সিনেমার ক্যাটেগরিতে ভারতীয় সিনেমার একমাত্র ‘অফিসিয়াল এন্ট্রির’—’সারাংশ’কে সর্বকালের অন্যতম সেরার স্বীকৃতি দিলেও, আশ্চর্য হতে হয় এই সিনেমার গান নিয়ে বিদ্বজ্জনদের মধ্যে তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য চর্চা বা আলোচনা না হওয়ায়।
এই সিনেমার সুরকার ছিলেন কলকাতার ছেলে অজিত বর্মণ, গীতিকার বসন্ত দেব। আশি দশকে বর্মণ-দেব জুটি বহু অবিস্মরণীয় গান উপহার দিয়েছেন বলিউডকে। যদিও পরবর্তীকালে খুব কম লোকই মনে রেখেছেন তাদের। ‘সারাংশ’-এ গানের সংখ্যা ছিল মাত্র দুটি। ভুপেন্দ্র সিং-এর কন্ঠে ‘আঁধিয়ারা গহরায়া’ ও অমিত কুমার-এর ‘হর ঘড়ি ঢল রহি হ্যায়’। দুটি গানই এককথায় অনবদ্য। সে বছর ‘সারাংশ’-এর জন্য সেরা গীতিকারের পুরস্কারও পান বসন্ত দেব। কিন্তু অজিত বর্মণ রয়ে যান বিস্মৃতির অন্ধকারে। ১৯৪৭ এর ২৬ মার্চ কলকাতায় জন্ম নেন প্রখ্যাত এই সুরকার। কাজ করেছেন সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, পঙ্কজ মল্লিক, সলিল চৌধুরীদের মতো কিংবদন্তিদের সঙ্গে। ষাটের দশকের গোড়াতেই সুরকার হিসেবে তিনি কাজ শুরু করেছিলেন। শুধু বাংলা চলচ্চিত্রেই নয়, বলিউডে-এও তার অবদান অবিস্মরণীয়। গোবিন্দ নিহালিনী, মহেশ ভাট-এর মতো প্রথম সারির নির্মাতাদের ছবিতে সুর দিয়েছেন তিনি। ‘বিজেতা’, আক্রোশ’, ‘সারাংশ’-এর মতো জনপ্রিয় বেশ কয়েকটি ছবির সুরকার ছিলেন বর্মন সাহেব। সিনেমায় ক্ল্যাসিকাল এবং সেমি-ক্ল্যাসিকাল মিউজিকের ‘ট্রিটমেন্ট’-এ ওই সময় তার মতো মুনশিয়ানা খুব কম সুরকারের ছিল। অথচ মানুষ তাকে মনে রাখেনি। মনে রাখেনি ‘বলিউড’ও। শেষ জীবনে পেয়েছিলেন ভয়াবহ একাকিত্ব ও অভাব। ২০১৬ সালের ১৫ ডিসেম্বর যখন মুম্বইয়ের আন্ধেরি হাসপাতালে একপ্রকার নিঃশব্দে চলে গেলেন অজিত বর্মণ, সে খবরও পেল না কেউ। এমনই দুর্ভাগ্য, তার শেষকৃত্যে চলচ্চিত্র জগতের কেউ হাজিরও ছিলেন না।
জীবনে অনেক দুঃখ, শোকের গান শুনেছি আমি। কিন্তু ‘সারাংশ’-এর এই গান ‘আঁধিয়ার গহরায়া’র মতো এত ‘ডার্ক, ‘গ্লুমি’ রচনা খুব কম পেয়েছি। কী অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য, অপার্থিব গভীরতা এই সুরে। ভূপেন্দ্র সিং-এর কন্ঠ গানটিকে পূর্ণতা দিয়েছে। বসন্ত দেব-এর রচনায় উঠে এসেছে দর্শনের সেই অমোঘ মৃত্যুত্তীর্ণ আলো, যা জীবনের অন্ধকার পথে আলোর দিশারী।
।। মিলে সুর মেরা তুমহারা।।
ফ্ল্যাশব্যাক ১
মহাসমুদ্র। অপার অশান্ত তরঙ্গ হিল্লোলিত। আস্তে আস্তে তা মুছে দেখা যায় ঝরনাধারা। কল্লোলিত মূর্চ্ছনা যুগের ওপার হতে নেমে আসছে পৃথিবীর বুকে। ক্রমশ তাকে ছাপিয়ে উঠে আসছে এক প্রাজ্ঞের মুখ। পণ্ডিত ভীমসেন যোশী। সিন্ধুভৈরবী রাগে ঝলমল করছে চারপাশ। তিনি গাইছেন—’মিলে সুর মেরা তুমহারা’।
ফ্ল্যাশব্যাক ২
শীতকালের ভোর। কুয়াশা মাখা রাস্তা ধরে হেঁটে আসছেন এক বৃদ্ধ। হঠাৎই দেখেন পথের একধারে এক ছোট্ট ছেলে বসে পোস্টার লিখছে। বৃদ্ধের মনে পড়ে গেল, ছেলেটির নাম কিষান, একদা নিরক্ষর, বৃদ্ধের সাহচর্যেই তার অক্ষরজ্ঞান। আজ সে নিজে নিজেই শব্দের মালা বুনছে। পরম মমতায় সেই বৃদ্ধ আদর করে দেন ছেলেটিকে। ছেলেটি হাসে। নির্মল সেই আলোর সারল্য-রোশনাই ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। নেপথ্যে তখন কবিতা কৃষ্ণমূর্তি, রাগ ভাটিয়ারে—’পূরব সে সুরজ উগা’।
ফ্ল্যাশব্যাক ৩
একঝাঁক ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়ের দল। বিকেলের পড়ন্ত আলো পিছনে ফেলে ছুটে আসছে। মিলিয়ে যাচ্ছে নৈর্ঋতে। ভেসে আসছে সেতার, পণ্ডিত রবিশঙ্কর। তারপর একে একে পণ্ডিত হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়া পণ্ডিত শিবকুমার শর্মা, উস্তাদ জাকির হুসেন উস্তাদ আল্লারাখা আমজাদ আলি খান-এর মতো প্রাতঃস্মরণীয়দের সমাহার। গায়নে বাদনে নৃত্যের তালে তালে উঠে আসছে দেশ রাগ। মন ছুঁয়ে যাওয়া সেই বন্দিশ—’বাজে সরগম হর তরফ সে…’
তখন আশি-নব্বই দশক। ৮৪’-র ভয়াবহতা কাটিয়ে দিল্লির মসনদে তখন রাজীব গান্ধির মৌরসীপাট্টা। টিভি সংস্কৃতি তখন সদ্য সদ্য ঢুকেছে বসার ঘরে। দূরদর্শন আর অল ইন রেডিও দাপিয়ে বেড়াচ্ছে পপুলার সার্কিটে। তখন ভারতীয় সোপ অপেরার স্বর্ণযুগ। আসমুদ্রহিমাচল মজে রয়েছে বি আর চোপড়ার ‘মহাভারত’ আর রামানন্দ সাগরের ‘রামায়ণ’-এ। উঠে আসছে ‘বুনিয়াদ’ (১৯৮৬-৮৭), ‘হামলোগ’ (১৯৮৪-৮৫), ‘সার্কাস’ (১৯৮৯-৯০), ‘নুক্কড়’ (১৯৮৬০৮৭), ‘গুল গুলশান গুলফাম’ (১৯৯১), ‘তমস’ (১৯৮৮), ফৌজি’ বা ‘মালগুড়ি ডেইজ’ (১৯৮৭)-এর মতো আরও বহু অবিস্মরণীয় সব টেলি-আখ্যান।
এহেন সময়ে ভারতীয় ঐক্য, সংহতি, সংস্কৃতি ও শিক্ষার প্রচারে নিয়োজিত কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সূত্র ধরে উঠে এল এই তিনটি ভিডিও, তিনটি সুর-রচনা। নয়া ইতিহাসের সৃষ্টি হল ভারতীয় টেলি জগতে। দূরদর্শন ও কেন্দ্রীয় তথ্যসম্প্রচার মন্ত্রকের উদ্যোগে ‘লোক সেবা সঞ্চার পরিষদ’ ও ‘জাতীয় সাক্ষরতা মিশন’-এর জনস্বার্থে প্রচারিত এই তিন সাংগীতিক কর্মশালা ‘মিলে সুরে মেরা তুমহারা’, ‘দেশ রাগ’ বা ‘পূরব সে সুরজ উগা’ আজও এমন মোহময়, মায়াবী এক সাংগীতিক কিংবদন্তি, যার জুড়ি মেলা ভার। ‘জন গণ মন’ ও ‘বন্দেমাতরম’-এর পর প্রায় ‘তৃতীয়’ জাতীয় সংগীতের সমান মর্যাদা পেয়েছিল ‘মিলে সুর মেরা তুমহারা’। পিছিয়ে ছিল না ‘দেশ রাগ’ বা ‘পূরব সে সুরজ উগা’ও। আজও এইসব শুনলে নস্ট্যালজিক হয়ে পড়েন না এমন মানুষ বিরল। কিন্তু মজার ব্যাপার, এই সুর রচনা তিনটি ক্রমেই কালোত্তীর্ণ হলেও এর রচনাকার বা সুরকাররা কিন্তু বিস্মৃতির আড়ালেই রয়ে গেছেন। অশোক পাটকি, লুই ব্যাংকস ও পীযুষ পাণ্ডেকে কতটাই বা মনে রেখেছি আমরা!
মহারাষ্ট্রের নাট্য, সিনেমা ও সংগীত জগতের দিকপাল ব্যক্তিত্ব অশোক পাটকি (জন্ম ২৫ আগষ্ট, ১৯৪১) প্রথম জীবনে হারমোনিয়ামবাদক হিসেবে খ্যাতিলাভ করলেও, নিজেও কখনও ভাবেননি কম্পোজার, অ্যারেঞ্জার হিসেবে বিখ্যাত হবেন। শৈশবে দিদি মীনা পাটকি (মারাঠি সিনেমার বিখ্যাত গায়িকা)-র অনুপ্রেরণায় প্রথম গান শিখতে বসা। হারমোনিয়াম বাদনে বিশেষ পারদর্শীতা লাভ করেন অশোক। নেন শাস্ত্রীয় সংগীতের তালিমও। সুমন কল্যাণপুর, পণ্ডিত জিতেন্দ্র অভিষেকী, সুধীর ফাড়কে-র সান্নিধ্যে কাটিয়েছেন বহু বছর। পরে শঙ্কর জয়কিষন, শচীন দেব বর্মণ ও রাহুল দেব বর্মণ-এর সহায়ক হিসেবেও বহু সিনেমায় মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্টের কাজ করেছেন। একশোরও বেশি মারাঠি নাটকে সংগীত পরিচালনার পাশাপাশি বানিয়েছেন বহু জিঙ্গল, সুরারোপ করেছেন মারাঠি-হিন্দি-কোঙ্কনি সিনেমাতেও। কোঙ্কনি সিনেমা ‘অন্তর্নাদ’ (১৯৯১)-এর জন্য পেয়েছেন সেরা সংগীত পরিচালকের জাতীয় পুরস্কার। আশি দশকের শেষভাগে ‘মিলে সুর মেলা তুমহারা’র সংগীত পরিচালকরূপে তিনি খ্যাতির শীর্ষে ওঠেন।
দার্জিলিং শহর থেকে পথ চলা শুরু ‘ভারতীয় জ্যাজ সংগীতের জনক’ লুই ব্যাংকস-এর। জন্ম ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১। গোর্খা পরিবারের ছেলে লুই ছোটোবেলা থেকেই ছিলেন ‘চাইল্ড প্রডিজি’। বাবা পুষ্কর বাহাদুরও ছিলেন একজন দক্ষ সংগীতজ্ঞ। তার কাছেই পিয়ানো, গিটার, ট্রাম্পেটের তালিম নেন লুই। যদিও তার আসল নাম দামবার বাহাদুর বুধাপ্রীতি, বিখ্যাত জ্যাজ শিল্পী ও ট্রাম্পেট-করোনেট বাদক লুই আমস্ট্রং-এর নামে রাখা হয় তার নাম। ওয়েস্টার্ন ক্লাসিকস, র্যেগে, জ্যাজ, ট্র্যান্স ও মেটালের পোকা লুই, বাবার পথ অনুসরণ করে আসেন কলকাতায়। বানান ‘লুই ব্যাংকস ব্রাদারহুড’ নামের ব্যান্ডটি। সেখান থেকেই রাহুল দেব বর্মণ-এর টিমে যুক্ত হয়ে ওয়ার্ল্ড ট্যুরের ডাক পান। বলিউড ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন ওতপ্রোতভাবে। বহু সিনেমা, জিঙ্গলে সংগীত পরিচালনা করলেও যন্ত্রানুসঙ্গ পরিচালনা মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্টে তার দক্ষতা ও মুনশিয়ানা ছিল প্রবাদপ্রতিম। আশি দশকের শেষে ‘মিলে সুর মেরা তুমহারা’, ‘দেশ রাগ’ ও ‘পূরব সে সুরজ উগা’-র সুর-সংযোজনা তাঁকে আলাদা করে প্রতিষ্ঠা দেয়।
‘অ্যাডম্যান’ পীযূষ পাণ্ডে-র কথা কে না জানে। ভারতীয় বিজ্ঞাপন ও বিপনন দুনিয়ার প্রাণপুরুষ পীযূষ পাণ্ডে-র জন্ম ১৯৫৫ সালে জয়পুরে। ছোটো থেকেই কবিতা, গল্প, সাহিত্যে ছিল তার প্রগাঢ় আকর্ষণ। নিজেও লিখতে পারতেন, আঁকতে পারতেন অসম্ভব ভালো। ছিলেন ভালো ক্রিকেটারও। জয়পুরের পাট চুকিয়ে দিল্লি এসে সেন্ট স্টিফেন্স কলেজ থেকে ইতিহাসে স্নাতক ও পরে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর পাস করেন। দেশের প্রথমসারির বিজ্ঞাপন সংস্থা ‘ওগলভি’তে চাকরি নেন তিনি। এরপরের ঘটনা অবশ্য ইতিহাস। ‘মিলে সুর মেরা তুমহারা’, ‘দেশ রাগ’ বা ‘পূরব সে সুরজ উগা’র মতো গানগুলির রচনা তাঁর হাতেই।
আমার মতো অসংখ্য মানুষ যাদের আশি-নব্বই দশকে জন্ম বা বেড়ে ওঠা, তাদের এই তিনটি কালজয়ী সৃষ্টির জন্য এই মানুষগুলির কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। নতুন করে চেনা উচিত, সম্মান করা উচিত এদের সম্মিলিত সৃষ্টিকে। যদিও আমরা আত্মবিস্মৃতের জাত। খুব সহজেই ভুলতে ভালোবাসি। তবু যে নস্টালজিয়া এই গানগুলি ঘিরে আমাদের বাঁচতে শেখায়, ভাবতে শেখায়, অনুপ্রাণিত হতে শেখায় সেই স্তরে অশোক পাটকি, লুই ব্যাংকস বা পীযূষ পাণ্ডে-র মতো মানুষরা আমাদের নির্ভেজাল আবেগের পরতে পরতে বেঁচে থাকবেন চিরকাল!
।। সুর সঙ্গম।।
নাট্যকার, সাহিত্যিক, মুক্তমনা গিরিশ কারনাডকে চিনেছি অনেক পরে। তারও আগে পরিচয় পণ্ডিত শিবশঙ্কর শাস্ত্রী-র সঙ্গে। অনেক পরে জেনেছি ‘তুঘলক’, ‘হায়াবদানা’, ‘নাগমন্ডলা’ বা ‘ওয়েডিং এলবাম’-এর রচনাকার কারনাড-কে, কিন্তু তারও আগে শুনেছি প্রবীণ সেই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতসাধকের কথা যিনি এক গণিকার মধ্যে খুঁজে ছিলেন রুদ্ধসংগীতের অশ্রুত আখ্যান।
১৯৮৫ সালের সেপ্টেম্বরে মুক্তি পেয়েছিল হিন্দি ছায়াছবি ‘সুর সঙ্গম’। তার পরিচালক দক্ষিণী চলচ্চিত্র জগতের নক্ষত্র কে বিশ্বনাথ। ১৯৮০ সালে তারই সুযোগ্য পরিচালনায় কিংবদন্তি তেলেগু ছায়াছবি ‘শঙ্করভরনম’-এর হিন্দি রিমেক হয়েছিল ‘সুর সঙ্গম’ নামে। গিরিশ কারনাড ছিলেন ছবিটির মুখ্য চরিত্রে, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতশিল্পী পণ্ডিত শিবশঙ্কর শাস্ত্রীর ভূমিকায়। ছিলেন জয়াপ্রদা, শচীন পিলগাঁওকর, গুফি পেইন্টাল-এর মতো অন্যান্য প্রতিভাবান কলাকুশলীরাও। তবে এই সিনেমার সবচেয়ে বড়ো সম্পদ গিরিশ কারনাড-এর অভিনয়, জয়াপ্রদার নাচ এবং অসাধারণ কিছু রাগাশ্রয়ী গান।
ভারতীয় চলচ্চিত্রে অন্যতম কাল্ট মুভি রূপে পরিচিত ‘শঙ্করভরনম’-এর মতই ‘সুর সঙ্গম’-এও ছিল অসামান্য কিছু রাগাশ্রয়ী ভজন, খেয়াল ও তারানার সমাহার। ‘শঙ্করভরনম’-এর সংগীতের দায়িত্বে ছিলেন দক্ষিণের বিখ্যাত সঙ্গীতকার কে ভি মহাদেবন। গান রচনার হাল সামলান ভি এস মূর্তি, মাইসোর বাসুদেবাচার্য-এর মতো প্রথিতযশা লিরিসিস্টরা। আর গানের দায়িত্বে ছিলেন এস পি বালসুব্রহ্মনিয়ম এবং বাণী জয়রাম-এর মতো শিল্পী। কর্ণাটকী ক্ল্যাসিকালে সমৃদ্ধ ছবিটি সেই বছর একাধিক জাতীয় সম্মানের মধ্যে জিতে নিয়েছিল বেস্ট মিউজিক, বেস্ট প্লে-ব্যাক মেইল ও বেস্ট প্লে-ব্যাক ফিমেলের খেতাব। কিন্তু ‘শঙ্করভরনম’-এর রিমেকে উত্তর ভারতীয় হিন্দুস্তানী শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রভাবকে বিস্তারিত করার সংকল্প নেন পরিচালক কে বিশ্বনাথ।
গিরিশ কারনাড অভিনীত ‘সুর সঙ্গম’-এর সংগীত পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন বলিউডের বিখ্যাত জুটি লক্ষ্মীকান্ত-প্যায়ারেলাল। গীতরচনায় বসন্ত দেব। প্লে-ব্যাকে ছিল রীতিমত অভিনবত্ব। গান গেয়েছিলেন পণ্ডিত রাজন-সাজন মিশ্র লতা মঙ্গেশকর কবিতা কৃষ্ণমূর্তি এস জানকী এবং সুরেশ ওয়াদেকর-এর মতো শিল্পীরা। পণ্ডিত শিবশঙ্কর শাস্ত্রীর চরিত্রে গিরিশ কারনাড-এর লিপে অধিকাংশ গানই গেয়েছিলেন রাজন ও সাজন মিশ্র। কর্ণাটকী ও হিন্দুস্তানী শাস্ত্রীয় গায়নে বিশারদ গিরিশ তার যথাযথ উপস্থাপনে দৃশ্যগুলির মানবৃদ্ধি ঘটান। ভূপালি, ভাটিয়ার, খাম্বাজ, দেশী ও পুরিয়া ধনশ্রীর মতো রাগাশ্রিত অনন্যসাধারণ সেই সব গান আজ তিন দশক পার করেও শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ রাখে। সে বছর ‘সুর সঙ্গম’-এর জন্য সেরা সংগীত পরিচালনার জাতীয় পুরস্কার জিতে নিয়েছিলেনলক্ষ্মীকান্ত-প্যায়ারেলাল।
মনে আছে, নব্বই দশকে দূরদর্শনে একাধিকবার প্রচারিত হয়েছিল গিরিশ অভিনীত ‘সুর সঙ্গম’। শুধুমাত্র সংগীতের জন্যই নয়, প্রবল প্রশংসিত হয়েছিল পণ্ডিত শিবশঙ্কর শাস্ত্রীর চরিত্রে গিরিশ কারনাড-এর অসামান্য অভিনয়। সংগীত সাধকের সেই চরিত্রে অসামান্য অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন কারনাড। তাঁর মৃত্যুতে এক মহীরুহ পতন হল ঠিকই, কিন্তু দুর্ভাগ্য যে আজও তাকে ‘এক থা টাইগার’-এর অন্যতম পার্শ্ব-চরিত্রাভিনেতা রূপে পরিচয় দেওয়া হয়। যারা এ তত্ত্বে বিশ্বাসী তাদের উচিত গিরিশ কারনাড অভিনীত ‘মন্থন’ (১৯৭৬), ‘স্বামী’ (১৯৮৭), ‘সংস্কার’ (১৯৮৭), ‘বংশ বৃক্ষ’ (১৯৭২), ‘নিশান্ত’ (১৯৭৫) বা ‘মালগুড়ি ডেইজ’ (১৯৮৭) দেখা। নিদেনপক্ষে দেখা উচিত কারনাড-এর অন্যতম মাস্টার পিস—’সুর সঙ্গম’ যা আমরা অনেকেই আজ ভুলে গেছি। যেখানে কারনাড ও পণ্ডিত শাস্ত্রীর চরিত্র যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। এখানেই তার সার্থকতা।
।। আফতাব-এ-মৌসিকি।।
সে বছর বরোদাতে ভয়াবহ গরম পড়েছিল। বর্ষা আসতে তখনও বহু দেরি। গোটা বরোদরা জ্বলছে অস্বাভাবিক তাপদাহে। দিনের বেলা তো বটেই, রাতেও এমন অস্বাভাবিক গরম যে মানুষ তিষ্ঠোতে পারছে না। সর্বত্র ত্রাহি ত্রাহি রব।
কথাসাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী তখন বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তিনি শাস্ত্রীয় সংগীতের বড়ো সমঝদারও বটে। তাঁরই বাড়িতে বসেছে মহ্যফিল। আসরের মধ্যমণি ‘আফতাব-এ-মৌসিকি’ উস্তাদ ফৈয়াজ খান সাহেব। তিনি তখন বরোদার মহারাজার সভাগায়ক। তামাম ভারতবর্ষ তাঁর সুরের জাদুতে মূহ্যমান। আলীসাহেবের সঙ্গে তার বিশেষ সখ্য। তাঁরই ডাকে সাড়া দিয়ে ফৈয়াজ খান এসেছেন গান শোনাতে।
আসরে উপবিষ্ট হয়ে শ্রোতাদের আদাব জানিয়ে খাঁ সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, আদেশ করুন কী শুনতে চান আপনারা। স্রোতাদের মধ্যে উঠল গুঞ্জন। কিছুক্ষণ পরে শলা পরামর্শ সেরে প্রায় সকলেই সমস্বরে আর্জি রাখলেন, গরমের এই প্রচণ্ড দাবদাহে সবাই কষ্ট পাচ্ছেন খুব। খাঁ সাহেব যদি মেহেরবানী করে কোনও বর্ষার গান শোনান তো ভালো হয়। এক মুহূর্ত চুপ করে ভাবলেন ফৈয়াজ খান। তারপর জলদ গম্ভীর কন্ঠে ধরলেন রাগ মেঘ মলহার।
খাঁ সাহেব সুর লাগাতেই গোটা সভা যেন মন্ত্রমুগ্ধ। ওদিকে খাঁ সাহেব তাঁর বিদ্যা, বোধ, রাগদারী, ভাব ও ঘরানার পেশকি উজাড় করে দিচ্ছেন। মনে হচ্ছে সভাগৃহে যেন সত্যি সত্যি একটু একটু করে ঘনিয়ে উঠেছে মেঘ, এমনই তাঁর কন্ঠের জাদু। প্রাচীন বন্দিশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যেন বইতে শুরু করেছে বৃষ্টির ঠান্ডা বাতাস। পালটাতে শুরু করেছে পরিবেশ। খাঁ সাহেবের সেদিকে হুঁশ নেই। চোখ বন্ধ করে মলহারকে নিংড়ে নিচ্ছেন তাঁর সুরের পরশে।
ঠিক এমন সময় ঘটলো সেই ‘অলৌকিক’ ঘটনা। সত্যি সত্যি কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি নেমে এল বরোদা শহরে। শ্রোতারা আনন্দে উচ্ছ্বাসে আত্মহারা। কেউ কেউ সেই বৃষ্টির মধ্যে নাচতে শুরু করেছেন, কেউ কেউ অবাক চোখে বাকরুদ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছেন খান সাহেবের দিকে, কেউ কেউ কেঁদে ফেলেছেন আবেগে। হাতজোড় করে খাঁ সাহেবকে বলছেন, আপনি মানুষ নন, সাক্ষাৎ ভগবান। সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ে জানাচ্ছেন অন্তরের শ্রদ্ধা।
শুধু খাঁ সাহেব নির্বিকার। গান শেষ করে চুপ করে বসে রইলেন। মাথা নিচু, চোখ বন্ধ, গালে হাত, ধ্যানস্থ। কী যেন ভাবছেন। মুখে কোনও কথা নেই। সেদিন মহ্যফিল শেষে একে একে সব অতিথি-অভ্যাগতরা বিদায় নিলে মুজতবা আলীর সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি বিদায় নিতে।
”আপনাকে এমন বিষণ্ণ লাগছে কেন খাঁ সাহেব?” প্রশ্ন করেন মুজতবা।
”এরা কি সবাই আমাকে ভগবান ভাবছে?” অস্ফুটে বলেন ফৈয়াজ। ”আমি তো সামান্য মানুষ। কিছুই গাইতে পারি না। ওস্তাদের আশীর্বাদ ও আল্লার মর্জিতে অতি সামান্য যেটুকু পারি, গাই। আপনি বলুন, আমার কি সত্যি ক্ষমতা আছে গান গেয়ে বৃষ্টি নামানোর?” হেসে ফেলেন মুজতবা। বলেন, ”আপনি গেয়েছেন বলে বৃষ্টি হয়েছে কিনা জানি না, তবে এটা জানি আল্লাতালহা আজ শুধু আপনার সম্মান রাখতে চেয়েছিলেন।”
প্রতিবছর গরমের শুরুতে এই পুরোনো গল্পটি মনে পড়ে। পুরোনো হলেও চর্চিত। সৈয়দ মুজতবা আলী তার লেখা ‘পঞ্চতন্ত্র’-এ এই ঘটনার উল্লেখ করেন। ‘কুদরত রঙ্গিবিরঙ্গি’তে এই অবিস্মরণীয় ঘটনাটির কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন পণ্ডিত কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এরপর বহু পত্রপত্রিকা, প্রবন্ধ, নিবন্ধেও স্থান পেয়েছে গল্পটি।
শুনলাম কলকাতায় বৃষ্টি হচ্ছে খুব। দিল্লিতে এখনও বৃষ্টি নেই। বাড়ছে গরম, ধুলোর ঝড়। শহর কলকাতা থেকে বহুদূরে এই রাজধানীতে অফিস ফেরতা মেট্রোতে শরীরের ক্লান্তি, ঘাম শুকোতে শুকোতে হঠাৎই মনে পড়ে গেল গল্পটি। গল্প হলেও সত্যি… চিরকালীন…শাশ্বত…
আমি জানি, আজ রাতে বৃষ্টি নামবে এই শহরেও। বর্ষা না হোক, ফৈয়াজি সুরের অবিশ্রান্ত বারিধারায় ভিজবে দিল্লি।
আমি সেই বৃষ্টিভেজা মাটির সোঁদা গন্ধ পাচ্ছি…
।। জানকীনাথ সহায়।।
তখন ২০০৩। প্রকাশ ঝা-এর ‘গঙ্গাজল’ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সারাদেশে। লোকের মুখে মুখে ঘুরছিল সেই ছবির ডায়লগ—’শালা, সব পবিত্র করে দেঙ্গে…’
সত্তর দশকের শেষের দিকে ঘটা কুখ্যাত ‘ভাগলপুর কাস্টডিয়াল ম্যাসাকার’ নিয়ে নির্মিত ‘গঙ্গাজল’ কুড়িয়েছিল সমালোচক ও দর্শকদের প্রশংসা। প্রকাশ ঝা-এর সিনেমা এমনিতেও ভালো লাগে। ‘দামুল’ (১৯৮৫), ‘মৃত্যুদণ্ড’ (১৯৯৭), ‘রাজনীতি’ (২০১০) বা নৃত্যশিল্পী সোনাল মানসিং-কে নিয়ে তার ডকুমেন্টারি ‘সোনাল’ (২০০১) গোগ্রাসে দেখেছি। ‘গঙ্গাজল’ও বেশ লেগেছিল। এস এস পি অমিত কুমারের চরিত্রে অজয় দেবগন এককথায় অসাধারণ। সিনেমাটি ছাড়াও আরও একজন আমায় প্রবল টেনেছিল, তিনি সারেঙ্গি বাদক উস্তাদ সুলতান খাঁ। সিনেমাটিতে তার গাওয়া দেড় মিনিটের একটি ছোট্ট পিস ছিল তুলসীদাসের ‘জব জানকীনাথ সহায় করে’। রাগ মিশ্র খাম্বাজ। বহু পরিচিত একটি ভজন। মনে আছে, সেই দেড় মিনিটের ধাক্কা সামলে উঠতে সময় লেগেছিল। এতদিন পণ্ডিত ডি ভি পালুস্কর আর শ্রীকৃষ্ণ রতনঝনকার ছিলেন এই ভজনটির ‘মিউচুয়াল শেয়ারহোল্ডার’। তাদের কন্ঠেই প্রথম শোনা। কিন্তু সেই প্রথম সুলতান খাঁ-র গলায় শুনি এই ‘রামধুন’। আর শুনেই এক ধাক্কায় সুরের ভাবসমাধি।
আর চার-পাঁচজনের মতো তার আগে থেকেই আমিও অবশ্য খান সাহেবের ভক্ত। উস্তাদ জাকির হুসেন-এর তবলার সঙ্গে তার স্বর্গীয় সারেঙ্গি বাদনের কথা না হয় বাদই দিলাম। ‘পিয়া বসন্তী রে’-গানটা আজও আমরা ভুলিনি। গানটিতে চিত্রা-র পাশাপাশি খাঁ সাহেবের সেই ‘ন্যাজাল ট্রিটমেন্ট’ আর কথায় কথায়, অনায়াসে তারসপ্তক ছুঁয়ে ছুঁয়ে আসা, ভিডিওর নায়িকা নৌহিদ কুরেশীর মতনই অলৌকিক সুন্দর মনে হয়েছিল। আর তারপর এই ভজন। যেমন ‘সুলতানি’ গায়কি, তেমনই তার ‘সারেঙ্গি’—দুইয়ের অভূতপূর্ব মিশেলে, যেন সুরের রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হল ‘গঙ্গাজল’ ছিটিয়ে।
তুলসীদাস ভজনে এমন অপার্থিব বিন্যাস আজও খুব কম চোখে পড়ে। ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়, আছে। উস্তাদ সুলতান খান নিঃসন্দেহে তার মধ্যে অন্যতম এবং অগ্রগণ্য। খাম্বাজ তার হারানো ‘বাজ’ খুঁজে পেল যেন সেই সুলতানি বিন্যাসে। আর আমাদের বুঁদ হয়ে থাকা ক্রমশই যেন অন্তহীন হয়ে ওঠে, আরও আরও…