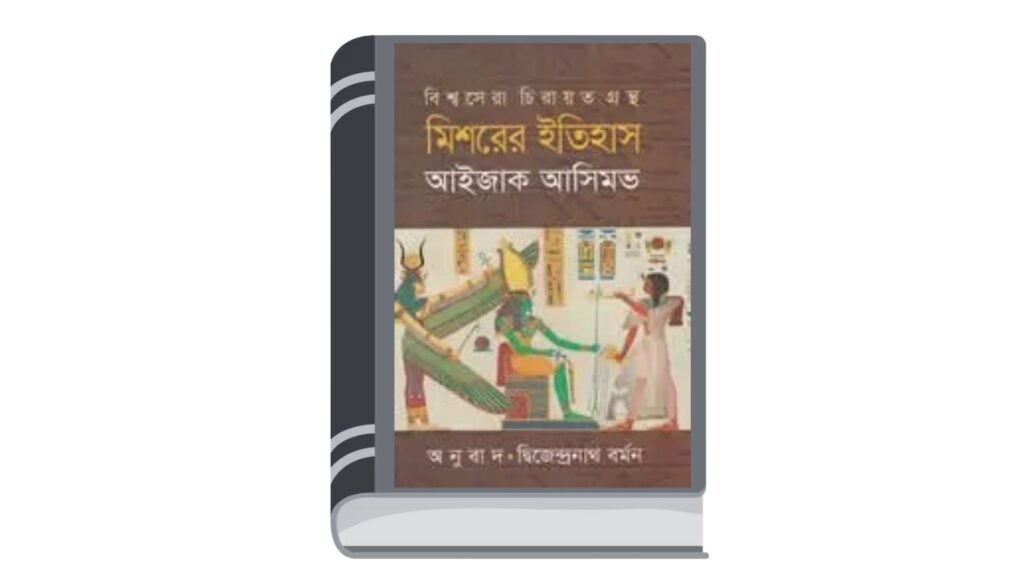১১. ক্লিওপেট্রা
১১. ক্লিওপেট্রা
জুলিয়াস সিজার
টলেমীয়দের দুর্বলতা ও বালখিল্যতা সত্ত্বেও মিশরীয়রা অর্ধ শতাব্দীব্যাপী শান্তির আবহ উপভোগ করেছিল। যে শান্তি ভঙ্গ হয়েছিল শুধু আলেক্সান্দ্রিয়ায়। কারণ সেখানে নির্দিষ্ট কিছু টলেমীয়দের উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল তারা যেন জাঁকজমকপূর্ণ মিশরীয় পোশাক পরিধান না করে, রাজকীয় কোনো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ না করে এবং মিশর রাজের ব্যয়বহুল রাজ্যাভিষেকে না যায়।
টলেমীয়রা অনায়াসে মিশরীয় সিংহাসন অধিকার করতে পেরেছিল কারণ যুদ্ধের বাতাবরণ তিরোহিত হয়েছিল। রোমানরা শুধু প্রাচ্যের অধিকার টিকিয়ে রাখতেই তাদের শক্তি ক্ষয় করছিল।
১৪৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মেসিডন রোমের একটি প্রদেশে পরিণত হয় এবং গ্রীসও পশ্চিমের এই মহান নগরীর আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়। ১২৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এশিয়া মাইনরের পশ্চিমাংশ রোমের প্রদেশে পরিণত হয় এবং উপদ্বীপের অবশিষ্টাংশ স্বাধীন হলেও এক ক্রীড়নক রাজ্যরূপে পরিগণিত হয়।
পূর্ব এশিয়া মাইনরের একটি রাজ্য পন্টাস যখন রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয় লাভ করে, রোম তখন তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে শেষ পর্যন্ত পূর্বাংশ সম্পূর্ণরূপে শত্রুমুক্ত রাখতে সক্ষম হয়। এই চূড়ান্ত সমাধানের কৃতিত্ত্ব যে রোমান জেনারেলের তার নাম নেউস পম্পেউস ইংরেজিতে যাকে বলা হয় পম্পেই। এয়োদশ এন্টিয়োকাসের অধীনে সেলুকীয় সাম্রাজ্যের শেষ চিহ্ন সিরিয়াতে সীমাবদ্ধ ছিল এবং ৬৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পম্পেই-এর আদেশে তা প্রদেশ হিসাবে রোমান সাম্রাজ্যের অধিভুক্ত করা হয়। টলেমীয় ও সেলুকীয়দের দেড় শতাব্দীব্যাপী যুদ্ধের অবসান হলো। ছয়টি মহাযুদ্ধে লড়াই করেছিল টলেমী দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং অষ্টম। সবকিছু আস্তাকুড়ে নিক্ষীপ্ত হয়েছিল! মেসিডোনীয়রা পরাজিত হয়েছিল এবং ভূঁইফোড় রোমানরাই বিজয় লাভ করেছিল। সিরিয়া ও জুডিয়া গ্রাস করা হয়েছিল।
টলেমীয়দের দূরবর্তী দেশগুলোকেও নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছিল। সপ্তম টলেমীর পুত্র ফাইসন যিনি সাইরেনির উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন, ৯৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মৃত্যুকালে তিনি তা রোমানদের নামে উইল করে দিয়েছিলেন এবং ৭৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এটি রোমের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। ৫৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সাইপ্রাস সর্বগ্রাসী রোমের উদরস্থ হয়।
আড়াই শতাব্দী পূর্বে মহান আলেক্সান্ডার বিজয়ের মাধ্যমে যে বিশাল এলাকা মেসিডনের জন্য অর্জন করেছিলেন, ৫৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ শুধু মিশরের নীল উপত্যকাতেই তার শেষ চিহ্ন টিকে থাকে। তবে এটাও ছিল রোমের ক্রীড়নক, কারণ বরামের অনুমতি ছাড়া টলেমীদের কেউই রাজা হতে পারত না। ঘটনাটি এ রকম যে, একাদশ টলেমী (অথবা সম্ভবত দ্বাদশ এয়োদশও, কারণ শেষ কয়েকজন টলেমীয়কে এই পর্যায়ে ছায়ামূর্তি বলে মনে করা যেতে পারে), যার দাপ্তরিক নাম ছিল টলেমী ডাইওনিসাস, তবে তিনি জনপ্রিয় ছিলেন টলেমী অলেটেস (বংশীবাদক টলেমী) নামে। কারণ তিনি বাঁশী বাজানোতে ওস্তাদ ছিলেন। তিনি ছিলেন অষ্টম টলেমীর (যিনি থিবিস ধ্বংস করেছিলেন) অবৈধ সন্তান, এবং যেহেতু কোনো বৈধ উত্তরাধিকারী ছিল না তাই তিনিই ছিলেন সিংহাসনের প্রত্যাশী।
৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি নিজেকে রাজা ঘোষণা করেন, তবে এই পদটি সুরক্ষিত রাখার জন্য তার রোমান সিনেটে অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল। এর জন্য প্রয়োজন ছিল একটি সুচিন্তিত এবং বিশাল অঙ্কের উৎকোচের। এ নিয়ে দরকষাকষিতে বহু বছর কেটে যায়। উৎকোচের অঙ্ক বাড়াতে তিনি কর বৃদ্ধি করেন আর এতে করে ক্ষিপ্ত হয়ে আলেক্সান্দ্রিয়ার লোকজন ৫৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়।
প্রতিবাদে তিনি রোমে আশ্রয় প্রার্থনা করেন যা ছিল তখন জেনারেল পম্পেইর অধিকারে। এবার অলেতেস আরও একটি উৎকোচের ঘোষণা দেন যদি রোমানরা তাকে সিংহাসন ফিরিয়ে দিতে পারে, আর তা হলো মিশরের কৃষকদের শেষ রক্তবিন্দু চুষে খাওয়া এবং মন্দিরসমূহের সম্পদ লুটপাট করা।
অর্থের ব্যাপারে রোমান নেতাদের তেমন অনীহা ছিল না এবং ৫৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে অলেতেসকে সিংহাসনে পুনঃস্থাপিত করা হয় যেটা অসহায় মিশরীয়দের চরম ঘৃণা ও ক্রোধের উদ্রেক করে। তিনি তার অবস্থান ধরে রাখতে পেরেছিলেন শুধু বৃহৎ এক নোমান দেহরক্ষী বাহিনীর মাধ্যমে আর এই রক্ষীবাহিনীর প্রধান ছিলেন পম্পেই। তবে ৫১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তার মৃত্যুর মাধ্যমে পৃথিবীকে রেহাই দিয়ে যান এবং তার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র দ্বাদশ টলেমীকে উত্তরাধিকারী রেখে যান। তিনি উইল করে তার পুত্রকে রোমান সিনেটের অধীন করেন এবং সিনেট তাকে অভিষিক্ত করে।
দ্বাদশ টলেমীর বয়স ছিল দশ বছর। তবে তিনি তার সতেরো বছর বয়স্কা ভগ্নির সহযোগিতায় দেশ শাসন করেন (এই ভ্রাতা-ভগ্নির যৌথ শাসন টলেমীয়দের জন্য নতুন কিছু নয়, কারণ দুই শতাব্দী পূর্বে এই ব্যবস্থা দ্বিতীয় টলেমীর ক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছিল যার ভগ্নি-পত্নী ছিলেন রানি আরসিনো)। বালক রাজার ভগ্নি একটি নাম ধারণ করেছিলেন, যেটি টলেমীয়দের একটি সাধারণ প্রচলন। অবশ্য তিনি এই নামধারীদের মধ্যে ছিলেন সপ্তম ব্যক্তি তাই তিনি পরিচিত ছিলেন সপ্তম ক্লিওপেট্রা নামে। তবে তিনি ক্লিওপেট্রা নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন, রোমান সংখ্যাটি তার নামের সাথে তেমন ব্যবহার হয় না (তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ক্লিওপেট্রার শরীরে কোনো মিশরীয়র রক্ত প্রবাহিত ছিল না। তার সমস্ত পূর্ব পুরুষরা ছিল হয় গ্রিক নয়তো মেসিডোনীও)।
টলেমীয় মহিলারা ছিলেন পুরুষদের চাইতে অধিকতর সক্ষম, আর বলা যেতে পারে ক্লিওপেট্রা ছিলেন সবার চাইতে অধিকতর সুদক্ষ। এটাই স্বাভাবিক যে, ষড়যন্ত্র-কন্টকাকীর্ণ দেশে সক্ষম বড় বোনের চাইতে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালককেই বেশি পছন্দ করা হবে, কারণ এই বড় বোনটিকে সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। বিশেষ করে যখন পথিনাস নামে এক খোঁজা সে সময় শাসনক্ষমতা দখলে রেখেছিল, আর সে ছিল এই নারীর একজন বিষাক্ত শক্ত।
৪৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ক্লিওপেট্রা মিশরকে এই সংকট থেকে বের করে আনার একটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন যেটি ছিল মিশরের জন্য একটি প্রচলিত পদ্ধতি। তিনি আলেক্সান্দ্রিয়ার বাইরে থেকে একটি সৈন্যবাহিনী সগ্রহ করতে চেয়েছিলেন আর এ জন্য তিনি সিরিয়াকে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি একটি গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে বিষয়টি সুরাহা করতে চেয়েছিলেন। তার এবং তার ভাইয়ের বাহিনী পেলুসিয়ামের যুদ্ধে পরস্পরের মুখোমুখি হয়, তবে প্রকৃত যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বেই এমন কিছু ঘটেছিল যাতে সবকিছু ওলটপালট হয়ে যায়।
সে সময় রোমেও একটি গৃহযুদ্ধ চলছিল। পম্পেই তখন মরিয়া হয়ে তার চাইতেও একজন অধিকতর ক্ষমতাশালী সেনাপতি জুলিয়াস সিজারের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। উভয় সৈন্য গ্রীসে পরস্পরের মুখোমুখি হয় আর এতে বিজয়ী হলেন সিজার। পম্পেইয়ের জন্য পলায়ন ছাড়া গত্যন্তর ছিল না, আর সাধারণভাবেই তিনি আশ্রয় প্রার্থনা করেন মিশরে (যেমনটা ঘটেছিল দুই শতাব্দীপূর্বে স্পার্টান ক্লিওমেনিসের ক্ষেত্রে)। মিশর ছিল কাছাকাছি জায়গা এবং নামমাত্র স্বাধীন। দেশটি ছিল দুর্বল কিন্তু সম্পদশালী আর একটি সেনাবাহিনী পুনর্গঠনে পম্পেইকে অর্থ সাহায্য দিয়েছিল। টলেমী অলেতেসেরও পম্পেইকে প্রয়োজন ছিল সিংহাসনে টিকে থাকার জন্য। আর তিনি অলেতেসের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী শিশু পুত্রের অভিভাবকরূপে কাজ করেছিলেন।
তবে পম্পেইয়ের জাহাজ মিশরীয় উপকূলের নিকটবর্তী হওয়ায় মিশরীয় রাজদরবার ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল। নিজেদের দেশে যখন গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার উপক্রম, তখন তারা রোমের গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণে উৎসাহী ছিল। যদি তারা পম্পেইকে সাহায্য করে তাহলে হয়তো সিজার ক্ষিপ্ত হয়ে ক্লিওপেট্রার উপর আক্রমণ চালাতে পারে। আবার যদি পম্পেইকে সাহায্য করতে অস্বীকার করে তাহলে তিনি হয়তো তাদের সাহায্য ছাড়াই জয়লাভ করবেন আর ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের উপর প্রতিশোধ নেবেন।
পথিনাস একটি উপায়ের কথা ভাবলেন। তিনি পম্পেইয়ের নৌবহরে একটি নৌকা পাঠিয়েছিলেন। পম্পেই মহা আনন্দে তাদের স্বাগত জানিয়েছিল এবং তাদেরকে তীরে আসতে আহবান জানিয়েছিল যাতে তিনি আলেক্সান্দ্রিয়ার জনগণের দ্বারা অভিনন্দিত হতে পারেন। তারপর যখন পম্পেই কূলে পা রাখলেন (নৌকা থেকে তার স্ত্রী ও পুত্র অবলোকন করছিল), তখন ঠান্ডা মাথায় তাকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করা হল।
এমনটাই হওয়ার কথা ছিল। পম্পেই এখন মৃত আর তাই কোনো প্রতিশোধ নিতে পারবে না। সিজারেরও কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত এবং তিনি নিশ্চয়ই ক্লিওপেট্রার সৈন্যের বিরুদ্ধে পথিনাসকে সাহায্য করবেন। এক ঢিলে দুই পাখি।
এর কয়েকদিন পরে চার হাজার সৈন্যের একটি ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে সিজার আলেক্সান্দ্রিয়ার উপকূলে অবতরণ করলেন। তিনি দৃঢ়-সংকল্প ছিলেন পম্পেইকে বন্দী করবেন, যাতে তিনি কোনো শক্তিশালী সেনাদল গঠন করতে না পারেন। তাছাড়াও সিজারের ইচ্ছা ছিল আলেক্সান্দ্রিয়ার সম্পদশালী দরবার থেকে কিছু অর্থসংগ্রহ করবেন।
পথিনাস অবিলম্বে পম্পেইয়ের খণ্ডিত মস্তক নিয়ে হাজির হলেন এবং ক্লিওপেট্রার বিরুদ্ধে সাহায্য চাইলেন। হয়তো এটা সম্ভব যে কিছু অর্থ পেলেই সিজার সেই সাহায্য প্রদান করবেন। কোন্ টলেমী মিশর শাসন করছে, তাতে তার কী যায় আসে?
তবে কেউই ক্লিওপেট্রাকে হিসাবের মধ্যে রাখল না। ক্লিওপেট্রার একটা বিশেষ সুবিধা ছিল, যেটা পথিনাসের ছিল না। তিনি ছিলেন সুন্দরী আকর্ষণীয়া যুবতী। কেউই জানেনা আধুনিক মাপকাঠিতে কতটা সুন্দরী ছিলেন তিনি অথবা তিনি মোটেই সুন্দরী ছিলেন কি না। কারণ তার কোনো ছবিই বর্তমানে পাওয়া যায়নি। তবে প্রশ্নতীতভাবে বলা যায় সুন্দরী হোক বা না হোক পুরুষদের আকৃষ্ট করার এক বিশেষ ক্ষমতা ছিল তার।
ক্লিওপেট্রার জন্য তাই প্রয়োজন ছিল তার ভাইয়ের সৈন্যদের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া আর সিজারের সামনে গিয়ে দাঁড়ানো। তাহলে তিনি নিশ্চিত হতে পারবেন যে, তাকে করায়ত্ব করা যাবে কি না। কাজেই সিরিয়া থেকে তিনি নৌযাত্রা করলেন এবং আলেক্সান্দ্রিয়ার উপকূলে গিয়ে অবতরণ করলেন এবং সেখানে গিয়ে সিজারকে একটি বিশাল কার্পেট উপহার দিলেন (প্রচলিত কাহিনী অনুসারে)। পথিনাসের সৈন্যবাহিনীরা এই উপহার প্রদানে আপত্তিকর কিছু দেখলো না, কারণ তারা জানতই না এই কার্পেটের মধ্যে জড়িয়ে রয়েছেন খোদ ক্লিওট্রো।
ক্লিওপেট্রার কৌশল পুরোপুরি কাজে লাগে। কার্পেট খোলা হলে সিজার মুগ্ধ বিস্ময়ে সেই সুন্দরী যুবতীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। ক্লিওপেট্রা তার আগমনের কারণ বোঝাতে সক্ষম হলেন। তাই তিনি আগের ব্যবস্থা পুনঃস্থাপন করতে আদেশ দিলেন। অর্থাৎ ক্লিওপেট্রা এবং তার বালক ভ্রাতা একত্রে শাসক হবেন।
এটা অবশ্য পথিনাসের জন্য পছন্দনীয় ব্যাপার ছিল না। তিনি জানতেন যে, মিশর সম্ভবত রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে টিকতে পারবে না, তবে সিজারের ক্ষুদ্র সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব। যদি সিজারকে হত্যা করা যায় তাহলে রোমে সিজারবিরোধীরা রোমের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেবে এবং সে ক্ষেত্রে পথিনাসও প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা লাভ করবে। পথিনাসের এমনটাই যুক্তি।
কাজেই তিনি সিজারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসলেন এবং তিন মাস যাবৎ রোমানরা ফায়োস দ্বীপে (যেখানে রয়েছে একটি লাইটহাউস) অবরুদ্ধ হয়ে রইল। সিজার টিকে রইলেন শুধু তার ব্যক্তিগত সাহসিকতা ও কুশলতা দিয়ে, যার সাহায্যে তিনি তার ক্ষুদ্র বাহিনীকে পরিচালিত করেছিলেন (এই ক্ষুদ্র যুদ্ধে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশাল লাইব্রেরি নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল)।
তবে পথিনাস নিজে যে সংকট সৃষ্টি করেছিলেন তা তার বিশেষ কোনো কাজে লাগেনি। যেই মুহূর্তে মিশরীয়রা আক্রান্ত হয় সেই মুহূর্তেই সিজার পথিনাসকে বন্দী করে হত্যা করেন।
অবশেষে সিজারের কাছে তার বর্ধিত জনবল পোঁছে গেল এবং মিশরীয়রা পরাজিত হল। মিশরীয়দের পলায়নের এক পর্যায়ে বালক দ্বাদশ টলেমী একটি প্রমোদতরীতে করে নীল নদের মধ্যদিয়ে পলায়নের চেষ্টা করে। তরীটিতে অত্যধিক যাত্রী উঠার কারণে সেটা ডুবে যায় আর এতেই তার পরিসমাপ্তি ঘটে।
এবার সিজার মিশরের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এলেন। সর্বজনীন প্রচলিত গল্প অনুসারে এবার তিনি এবং ক্লিওপেট্রা পরস্পরের প্রেমিক প্রেমিকা, আর এভাবেই ক্লিওপেট্রা তার সিংহাসন ধরে রাখার চেষ্টা করেন। যা হোক, একজন রানির পক্ষে তার একজন সহচর অপরিহার্য। আর সেই উদ্দেশ্যে সিজার ক্লিওপেট্রার আর এক ছোট ভাইকে ব্যবহার করলেন। তিনি ছিলেন দশ বছর বয়স্ক এক বালক যিনি ত্রয়োদশ টলেমীরূপে দেশ শাসন করেন।
সিজার চিরকাল মিশরে থাকতে পারেন না। এশিয়া মাইনরে রোমানদের বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধ চলছিল যেটার সুরাহা করা প্রয়োজন। পশ্চিম আফ্রিকা এবং স্পেনে তখনও পম্পেইয়ের বিশ্বস্ত সেনাবাহিনী রয়ে গিয়েছিল এবং তাদের মোকাবেলা করা দরকার। তার চাইতেও বড় কথা রোমের সরকারব্যবস্থা সংস্কার ও পুনর্গঠন করা প্রয়োজন। তাই ৪৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি মিশর থেকে নৌযাত্রা করে রোমে ফিরে এলেন।
সিজার সাথে করে রোমে কিছু একটা নিয়ে এলেন। তিনি মিশরে এক পঞ্জিকা দেখেছিলেন যেটা ছিল সূর্য-কেন্দ্রিক যা রোম ও গ্রীসে প্রচলিত চান্দ্র-পঞ্জিকা থেকে অধিকতর উপযোগী।
তিনি সসিজিনেস নামে একজন আলেক্সান্দ্রীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীর সাহায্য চেয়েছিলেন এবং রোমে একটি অনুরূপ পত্রিকা প্রবর্তন করেছিলেন। এই পঞ্জিকায় ছিল বৎসরে ১২টি মাস এবং প্রতিটি মাস ৩০ ও ৩১ দিনের। এটা অবশ্য মিশরীয় পঞ্জিকার মতো সমসংখ্যক ৩০ দিনের মাস ছিল না, যার শেষ মাসটি ছিল ৩৫ দিনের। তবে মিশরীয়রা এই পরিবর্তন কখনো গ্রহণ করেনি। যেহেতু প্রতিটি বছর ছিল ৩৬৫.২৫ দিনের, ৩৬৫ দিনের নয়, তাই প্রতি চার বছর পরপর একটি অতিরিক্ত দিন যোগ করতে হয়। এটাকে বলে “জুলিয়ান ক্যালেন্ডার” (জুলিয়াস সিজারের নাম অনুসারে)। এর ছয়শত বছর পরে ক্যালেন্ডারে সামান্য একটু পরিবর্তন যোগ হয় যেটা এখন পর্যন্ত প্রচলিত আছে। কাজেই আমাদের পঞ্জিকা সরাসরি মিশরের সাথে যুক্ত, যেটা জুলিয়াস সিজারের স্বল্পকালীন মিশরে অবস্থানের ফসল।
সিজারের প্রত্যাবর্তনের অল্পদিনের মধ্যেই ক্লিওপেট্রার এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তার নাম দেওয়া হয় টলেমী সিজার এবং তার ডাকনাম সিজারিয়ন (ছোট্ট সিজার)।
.
মার্কএন্টনি
রোমে প্রত্যাবর্তনের পর সিজারের জীবন ছিল সংক্ষিপ্ত। তার বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র দানা বাঁধতে থাকে আর ৪৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তাকে হত্যা করা হয়। সিজারের মৃত্যুর পরপরই ক্লিওপেট্রা তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ত্রয়োদশ টলেমীকে হত্যা করান। কারণ তার অস্বস্তিকর বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটছিল- ইতিমধ্যে তার বয়স হয়েছিল চৌদ্দ বছর এবং শাসনকার্যে তিনি ভূমিকা রাখতে শুরু করেছিলেন। ক্লিওপেট্রা এবার তার পুত্র টলেমী সিজারের (সে সময় তার বয়স তিন বছরের চেয়েও কম) সাথে যৌথভাবে শাসনকার্য পরিচালনা শুরু করেন, যার উপাধি ছিল চতুর্দশ টলেমী।
ইতিমধ্যে রোমে দুজন ব্যক্তি ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করায় ধীরে ধীরে শৃঙ্খলা ফিরে আসছিল। এর মধ্যে একজন হলেন মার্কাস এন্টনিয়াস, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় মার্ক এন্টনি। তিনি ছিলেন সিজারের একজন বিশ্বস্ত সহযোদ্ধা। অন্যজন হলেন অক্টেভিয়ান সিজার, যিনি ছিলেন জুলিয়াস সিজারের নাতি (ভাগ্নের পুত্র)।
এই দুই ব্যক্তি আপাত শক্ত হলেও পরস্পরের সাথে আপোস করতে সম্মত হয়েছিলেন। যে আপোসের ফলে রোমান এলাকায় বাইরের কোনো প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা দূরীভূত হলো। অক্টেভিয়ানের অধিকারে চলে গেল রোম নগরীসহ রাজ্যের পশ্চিম অংশ আর মার্ক এন্টনির অধিকারে রইল পূর্বাঞ্চল।
এই বিভাজনের প্রকৃতিই দুই ব্যক্তির প্রকৃতি নির্দেশ করে। মার্ক এন্টনি ছিলেন আকর্ষণীয়, হাস্যোজ্জ্বল, পানাসক্ত এবং তিনি লোকজনের সাথে পানভোজন উপভোগ করতেন। তার সক্ষমতা সত্ত্বেও তিনি ঠান্ডা মাথায় যুক্তিপূর্ণ পরিকল্পনা করতে পারদর্শী ছিলেন না এবং সাময়িক আবেগতাড়িত হয়ে পড়তেন। রোম সাম্রাজ্যের পূর্বাংশ ছিল অধিকতর সভ্য ও সমৃদ্ধ। এখানে মার্ক এন্টনি আশা করতে পারতেন আরাম আয়েস ও বিলাসিতা।
মার্ক এন্টনি অক্টেভিয়ানকে সাংঘাতিকভাবে অবমূল্যায়ন করেছিলেন। সাধারণত ঐতিহাসিকরা শীতল অকৌতুকপ্রিয় অষ্ট্রেভিয়ানের চাইতে রোমান্টিক মার্ক এন্টনিকে অধিকতর আনুকূল্য দেখিয়েছেন তবে এ ব্যাপারে তাদের অবস্থান ভুল ছিল। দু হাজার বছরের পুরনো ইতিহাসের এই কালটির প্রতি যদি আমরা দৃষ্টি দিই তাহলে দেখতে পাব অক্টেভিয়ানই ছিলেন রোমান ইতিহাসে যোগ্যতম ব্যক্তি। এমনকি জুলিয়াস সিজারও এর আওতা থেকে বাদ পড়েন না। যদিও পিতামহের সমতুল্য সামরিক প্রতিভা তার ছিল না।
যে চক্রটি জুলিয়াস সিজারকে হত্যা করেছিল, ৪২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মেসিডনের যুদ্ধে তারা পরাজিত হয়। তারপর মার্ক এন্টনি জাহাজে করে তার পূর্ব সাম্রাজ্যে ফিরে যান। সেখানে তিনি এশিয়া মাইনরের দক্ষিণ উপকূলে ভাসাস নগরকে তার শাসন কেন্দ্রে পরিণত করেন।
এন্টনির প্রধান চহিদা ছিল অর্থ, যার সরবরাহ সর্বদা আসত মিশর থেকে। তাই তিনি রাজকীয় ভঙ্গিতে মাঝে মাঝে ক্লিওপেট্রাকে তাসাসে আসার আমন্ত্রণ জানাতেন এবং সিজারের মৃত্যুর পর সেখানকার শাসন-নীতি নিয়ে আলোচনা করতেন। অবশ্য মিশর সবসময় চেষ্টা করত এ সব ঘোরপ্যাঁচ থেকে দূরে থাকার এবং নিরপেক্ষতা বজায় রাখার, কারণ তারা জানত না কোন্ পক্ষ শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে। প্রকৃতপক্ষে এটা কোনো দোষের বিষয় ছিল না, তবে যে কেউ এটাকে অপরাধ ভাবতে পারত।
ক্লিওপেট্রার হাতে তখনও সেই ট্রাম্পকার্ড ছিল যেটা তিনি সাত বছর আগে জুলিয়াস সিজারের বিরুদ্ধে ছুঁড়েছিলেন। তিনি এক বিলাস সাজে সজ্জিত জাহাজে করে তার্সাসে এলেন। সে বিলাসিতার মাত্রা ছিল অকল্পনীয়। আর এই জাহাজে সবচেয়ে মূল্যবান সামগ্রীটি ছিলেন তিনি নিজে, তার বয়স তখনও মাত্র আটাশ বছর। জুলিয়াস সিজারের মতো মার্ক এন্টনিও এই সম্মোহনকারিণীর মোহে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন।
জুলিয়াস সিজার যেখানে কখনো তার ভালোবাসাকে শাসননীতির উপরে স্থান দেননি, সেখানে মার্ক এন্টনি কখনোই তার শাসন নীতিকে ভালোবাসার কবল থেকে মুক্ত করতে পারেননি।
রোমান জেনারেল ও মিশরীয় রানির এই মুখরোচক কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমকাহিনীরূপে, এর সবচেয়ে বড় কারণ হলো এর একটি বিষাদময় পরিসমাপ্তি রয়েছে। এই দুই প্রেমিক প্রেমিকা যুগল ভালবাসার জন্য সবকিছু বিসর্জন দিয়েছিলেন। শেক্সপিয়ার এই যুগলের প্রেম কাহিনীকে তার এন্টনি ও ক্লিওপেট্রা নাটকে অমর করে রেখে গেছেন এবং ইংরেজ কবি জন ড্রাইডেন তার কবিতায় প্রকাশ করেছেন এভাবে সব কিছু প্রেমের জন্য, নয়তো হারিয়ে যাবে পৃথিবী।
যদিও সন্দেহ নাই যে এই দুই ব্যক্তির মধ্যে গভীর প্রণয়-সম্পর্ক ছিল তবে সেটা সম্পূর্ণরূপে রোমান্স কেন্দ্রিক ছিল বলে মনে হয় না। ক্লিওপেট্রার ছিল অর্থ-সম্পদ আর মার্ক এন্টনির সেটির প্রয়োজন ছিল। ক্লিওপেট্রা বারো বছর ধরে সেই অর্থ যুগিয়ে গেছেন যার ফলে মার্ক এন্টনির পক্ষে ক্ষমতায় টিকে থাকা সম্ভব হয়। আর মার্ক এন্টনির ছিল সৈন্যবল যার প্রয়োজন ছিল ক্লিওপেট্রার। মিশরের রানি হিসেবে টিকে থাকার জন্য ঠান্ডা মাথায় ক্লিওপেট্রা সে বাহুবলকে কাজে লাগাতে পেরেছিলেন।
৪১-৪০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের শীতকালটি এন্টনি কাটিয়েছিলেন আলেক্সান্দ্রিয়ায় ক্লিওপেট্রার সাহচর্যে, যে সময় তিনি আমোদ-আহ্লাদে মত্ত ছিলেন। অবশেষে ক্লিওপেট্রা তার ঔরষে জমজ সন্তানের জন্ম দেন। মার্ক এন্টনিও সানন্দে তাদের গ্রহণ করেন এবং তাদের নাম দেওয়া হয় আলেক্সান্ডার হেলিওস এবং ক্লিওপেট্রা সেলিনি (আলেক্সান্ডার সূর্য এবং ক্লিওপেট্রা চন্দ্র)।
কিছুদিনের জন্য এই দুই প্রেমিক প্রেমিকার বিচ্ছেদ ঘটে তবে এন্টনি আবার ফিরে এসে ক্লিওপেট্রাকে বিবাহ করেন। যদিও প্রকৃতপক্ষে তিনি রোমে এসে অক্টেভিয়ানের ভগ্নিকেও বিবাহ করেছিলেন। তিনি ঠান্ডা মাথায় তার নোমান পত্রীকে বিবাহ বিচ্ছেদের নোটিশ পাঠান।
রোমে অক্টেভিয়ান এন্টনির এই বালখিল্যতার সুযোগ নিয়েছিলেন। তিনি বোঝাতে পেরেছিলেন এন্টনি কতটা নির্বোধ অকালকুষ্মাণ্ড। রোমের জনগণ এটাকে গ্রহণ করেছিল। তারা আরও অনুভব করেছিল অক্টেভিয়ান রোমের জন্য কতটা শ্ৰমস্বীকার করেন। তিনি অত্যন্ত মিতব্যয়ী, নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন করতেন এবং রোমের একটি ভদ্র পরিবারে বিবাহ করেছিলেন।
মার্ক এন্টনি এসব জনমতের খুব কমই মূল্য দিতেন। তার মতে অক্টেভিয়ান ছিলেন একজন অক্ষম জেনারেল এবং তিনি নিজে কুশলী যোদ্ধা (তবে তিনি যেটা ভাবতেন সেটা সম্পূর্ণ সঠিক নয়)। তাই এন্টনি তার নিজের পথে চলতেন আর কে কী ভাবছে তার মোটেই তোয়াক্কা করতেন না।
ক্লিওপেট্রা চেয়েছিলেন তার পূর্বপুরুষের বিস্তৃত সাম্রাজ্য ধরে রাখার। আর এ নিয়ে মার্ক এন্টনি তাকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতেন। এন্টনি তাকে সাইরেনি ও সাইপ্রাস ফিরিয়ে দিয়েছিলেন (যেটা করার তার কোনো অধিকার ছিল না)। এমনকি সিরিয়া ও এশিয়া মাইনরের উপকূলীয় অঞ্চলের বিস্তৃত এলাকা যা, এক সময় তৃতীয় টলেমীর অধিকারে ছিল সেটাও ক্লিওপেট্রাকে উপহার দেন। এটাও প্রবাদ আছে তিনি ক্লিওপেট্রাকে “পার্গে” নামের লাইব্রেরি (পশ্চিম এশিয়া মাইনরের একটি শহর যেখানকার গ্রন্থ-সংগ্ৰহ আলেক্সান্দ্রিয়ার কাছাকাছি ছিল) দান করেছিলেন।
অক্টেভিয়ানের জন্য এ সবকিছুই অপপ্রচারের কাজে লেগেছিল। তিনি জনগণকে বোঝাতে পেরেছিলেন যে এন্টনিও তার প্রেমিকার জন্য সব কিছুই বিলিয়ে দিতে পারেন। এমনও গুজব আছে যে সমগ্র প্রাচ্য অঞ্চল তিনি ক্লিওপেট্রাকে এবং তার উত্তরাধিকারী হিসেবে তার ছেলেমেয়েদের নামে উইল করে যান। এতে রোমানরা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠে যে একজন মেসিডোনীও রানি সবকিছু গ্রাস করছে শুধু তার সৌন্দর্যের আকর্ষণে। যেটা কোনো মেসিডোনীও রাজাও সক্ষম হননি বাহুবলে জয় করতে।
রোমান জনগণের ঘৃণা ও ক্রোধকে পুঁজি করে অক্টেভিয়ান সমর্থ হয়েছিলেন মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় সিনেটের সমর্থন আদায় করতে। যে যুদ্ধটি ছিল প্রকৃতপক্ষে মার্ক এন্টনির বিরুদ্ধে।
মার্ক এন্টনি নিজেকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। তখনও তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে অক্টেভিয়ানকে সহজেই পরাজিত করতে পারবেন। তিনি জাহাজ সংগ্রহ করে গ্রীসের দিকে অগ্রসর হলেন আর সে দেশের পশ্চিম অঞ্চলে তার হেড কোয়ার্টার স্থাপন করে ইতালি আক্রমণের প্রস্তুতি নিলেন। প্রথম উদ্যোগেই তিনি রোম দখল করে নিলেন।
অক্টেভিয়ান যদিও মোটেই দক্ষ সেনাপতি ছিলেন না, তবে তার কিছু অনুগত দক্ষ সেনাধ্যক্ষ ছিল। এদের মধ্যে একজন হলেন মার্কাস ভিস্পেনিয়াস আগ্রি। আগ্রিপ্পার অধীনে অক্টেভিয়ানের নৌবহর পশ্চিম গ্রীসের জলসীমায় প্রবেশ করল। অনেক আয়োজন প্রস্তুতির পর ক্লিওপেট্রা এন্টনিকে একটি নৌযুদ্ধে এগিয়ে যেতে তাগিদ দিল। এন্টনির জাহাজসমূহ সংখ্যায় এবং আয়তনে অক্টেভিয়ানের চাইতে অনেক বড় ছিল। যদি এন্টনি নৌযুদ্ধে জয়ী হতেন তাহলে এন্টনির পদাতিক বাহিনীও যেহেতু সংখ্যায় অনেক বেশি ছিল, সেহেতু চূড়ান্ত বিজয় এন্টনিরই হতো।
৩১ খ্রিস্টপূর্বাব্দের ২ সেপ্টেম্বর, পশ্চিম গ্রীস উপকূলে এষ্টিয়াম নামে এক শৈলান্ত রীপে যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। প্রথমে যদিও অক্টেভিয়ানের জাহাজসমূহ এন্টনির বিশাল যুদ্ধ জাহাজের সামনে মোটেই কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছিল না তবে এগ্রিপ্পার জাহাজসমূহ দ্রুতগতিতে এন্টনির জাহাজের মধ্যদিয়ে ক্লিওপেট্রার ষাটটি জাহাজ পিছনে ফেলে এগিয়ে যায়।
কাহিনীটা এরকম যে আতঙ্কগ্রস্ত ক্লিওট্রো তার জাহাজসমূহ নিয়ে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হন। এন্টনিও যখন বুঝতে পারেন যে ক্লিওপেট্রা এবং তার জাহাজসমূহ যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে যাচ্ছে, এন্টনিও তার জীবনের সবচেয়ে নির্বুদ্ধিতার কাজটি করে বসেন। তিনি ছোট একটি নৌকায় চড়ে তার রাজকীয় নৌবহর এবং সৈন্য সামন্তকে (যারা হয়তো তাকে বিজয় এনে দিতে পারত) পিছনে ফেলে রানির সঙ্গে পলায়নে যোগ দিলেন। তার পরিত্যক্ত নৌবহর প্রাণান্ত চেষ্টা করেছিল কিন্তু সেনাপতির অনুপস্থিতিতে তারা সাহস হারিয়ে ফেলে এবং শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করেন অক্টেভিয়ান।
.
সর্বশেষ টলেমীয়
আলেক্সান্দ্রিয়ায় অলস কালক্ষেপণ ছাড়া এন্টনি ক্লিওপেট্রার আর কিছুই করার ছিল না। তারা অপেক্ষা করছিল অষ্ট্রেভিয়ান মিশরে অদের পিছু ধাওয়া করতে আসে কি। ৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে জুলাই মাসে অক্টেভিয়ান তাই করলেন এবং পেলুসিয়ামে এসে হাজির হলেন। এন্টনি তাকে প্রতিরোধের চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। ১ আগষ্ট অক্টেভিয়ান আলেক্সান্দ্রিয়ায় প্রবেশ করলেন আর আত্মহত্যা করলেন মার্ক এন্টনি।
এবার ক্লিওপেট্রা একা। তখনও রয়েছে তার সৌন্দর্য, তার আকর্ষণ। তিনি আশা করলেন অক্টেভিয়ানের উপর এটা প্রয়োগ করবেন যেমন করেছিলেন সিজার ও এন্টনির উপরে। এখন তিনি উনত্রিশ বছর বয়স্কা। তবে এটা তেমন বেশি বয়স নয়।
অক্টেভিয়ান তার চেয়ে মাত্র ছয় বছরের ছোট, তবে সেটা ধর্তব্যের বিষয় নয়। আসল সমস্যা হল অক্টেভিয়ানের একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল, আর তা হলো রোমের পুনর্গঠন, এর সরকারের স্বীকৃতি আর এমন সুদৃঢ়ভাবে ভিত নির্মাণ করেন যাতে বহু শতাব্দীব্যাপী এর অস্তিত্ব টিকে থাকে (এর সবকিছুই তিনি সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন)।
এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য রানি ক্লিওপেট্রার আকর্ষণ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতেই হবে। রানির সাথে প্রথম সাক্ষাৎকারেই প্রমাণ হয়ে যায় তিনি এসবের উর্ধ্বে। তিনি রানির সাথে কোমল কণ্ঠে কথা বললেও রানির বুঝতে বাকী রইলনা যে মানসিকভাবে অক্টেভিয়ান কতটা কঠোর। রানি বুঝতে পারেন অক্টেভিয়ানের আসল উদ্দেশ্য তাকে শান্ত রেখে বন্দী করে রথের চাকায় বেঁধে টেনেহিঁচড়ে রোমে নিয়ে যাওয়া।
এই অবমাননার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার একটি মাত্র উপায় আত্মহত্যা। তিনি সম্পূর্ণ আনুগত্যের ভান করলেন এবং মনে মনে পরিকল্পনা স্থির করলেন। দূরদর্শী অক্টেভিয়ান এই সম্ভবনাটি অনুধাবন করতে পারলেন আর রানির কক্ষ থেকে সমস্ত তৈজস ও বিপজ্জনক জিনিসপত্র সরিয়ে ফেললেন। তৎসত্ত্বেও রোমান সৈন্যরা যখন তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য রানির কক্ষে উপস্থিত, তারা দেখতে পেল রানি মরে পড়ে আছেন।
যেমন করেই হোক রানি আত্মহত্যার একটা ব্যবস্থা করেই ছাড়লেন আর অক্টেভিয়ানের চরম বিজয়োল্লাস থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন। কিভাবে তিনি এটা করলেন কেউ জানতে পারেনি। তবে কাহিনী প্রচলিত আছে যে, তিনি একটি বিষাক্ত সাপকে (এস্প বিষধর ক্ষুদ্র সর্পবিশেষ) কাজে লাগিয়েছিলেন। এটা গোপনে ডুমুরের বাক্সে করে তার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই ঘটনাটিই ছিল তার জৌলুসময় জীবনের সবচেয়ে চমকপ্রদ অধ্যায়।
মিশরকে রোমের একটি প্রদেশে পরিণত করা হল। তবে প্রকৃতপক্ষে মিশর হয়ে পড়ে অক্টেভিয়ানের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার বাসনা নিয়ে, বর্তমানে যাকে আমরা বলি রোমান সাম্রাজ্য। তিনি অগাস্টাস উপাধি ধারণ করে প্রথম সম্রাটরূপে রোমের সিংহাসনে আরোহণ করেন।
আলেক্সান্ডার দ্য গ্রেটের মৃত্যু এবং প্রথম টলেমীর সিংহাসনে আরোহণের পর থেকে তিন শতাব্দীব্যাপী মিশরে টলেমীয় শাসনের অবসান ঘটল।
তবে ক্লিওপেট্রার মৃত্যুতে টলেমী বংশের অবসান ঘটেনি। নিশ্চিত করে বলা যায় অক্টেভিয়ান ঠান্ডা মাথায় রানির দুই শিশুপুত্র সিজারিয়ন ও আলেক্সান্ডার হেলিয়সকে হত্যা করেন, যাতে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কোনো বীজ অবশিষ্ট না থাকে। কিন্তু এন্টনি ও ক্লিওপেট্রার কন্যা ক্লিওপেট্রা সেলিনি তখনও বেঁচে ছিলেন।
অক্টেভিয়ান দশ বছর বয়েসী এক শিশু কন্যাকে হত্যা করাকে তেমন আবশ্যক মনে করেননি, তবে তিনি স্থির করেন মেয়েটিকে বিবাহ দিয়ে পৃথিবীর কোনো দূর প্রান্তে সরিয়ে দেওয়ার, যাতে তার পক্ষ থেকে কোনো বিপদের আশঙ্কা না থাকে। তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় নুমিডীয় (এই স্থানটি বর্তমানে আলজেরিয়ার অন্তর্গত) রাজার পুত্র জুবার দিকে।
অক্টেভিয়ান ভেবেছিলেন জুবা ব্যক্তিটিই হবে ক্লিওপেট্রার কন্যার কবর। জুবার সাথে বিয়ে হয়ে যায় ক্লিওপেট্রা সেলিনির। তিনি দ্বিতীয় জুবা নামে তার পিতার সিংহাসনে আরোহণ করেন। কয়েক বছর পরে অগাষ্টাস (যিনি অক্টেভিয়ান নামে পরিচিত ছিলেন) স্থির করলেন নুমিডীয়াকে রোমান সাম্রাজ্যের প্রদেশে পরিণত করাই সঙ্গত হবে এবং তিনি জুবা এবং তার স্ত্রীকে পশ্চিম দিকে মৌরিতানিয়ায় (বর্তমানে মরক্কো) পাঠিয়ে দিলেন। যেখানে তারা রোমের ক্রীড়নক হিসেবে শান্তিতে রাজত্ব করেন।
অধিকন্তু তাদের ছিল এক পুত্র যাকে বংশধারার প্রতীক হিসাবে নাম দিয়েছিল টলেমী, যিনি ইতিহাসে পরিচিত টলেমী মৌরিতানিয়া নামে। ক্লিওপেট্রার এই নাতিটি (অগাষ্টাসের মৃত্যুর চার বছর পর) ১৮ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং একুশ বছর ধরে শান্তিপূর্ণভাবে রাজত্ব করেন।
৪১ খ্রিস্টাব্দে রোম চলে আসে তৃতীয় ম্রাট ক্যালিগুলার অধীনে। ক্যালিগুলা ছিলেন অগাষ্টাসের মায়ের দিক থেকে তার নাতির ছেলে। তিনি বেশ ভালোভাবেই তার শাসনকার্য শুরু করেন। তবে একটা অসুখে ভুগে তিনি উন্মাদ হয়ে যান। তার অমিতব্যয়িতা চরম শিখরে পৌঁছে এবং তিনি চরম অর্থ সংকটে পড়েন। যখন এমনটা ঘটছিল মৌরিতানিয়ায় টলেমী তার সম্পদ খুব সতর্কভাবে রেখেছিলেন। ক্যালিগুলা একটা বাজে অজুহাত দিয়ে তাকে রোমে ডেকে পাঠান এবং হত্যা করেন। মৌরিতানিয়াকে রোমের একটি প্রদেশে পরিণত করা হয় আর মৌরিতানিয়ার সব ধনসম্পদ ক্যালিগুলা হস্তগত করেন। এভাবেই ক্লিওপেট্রার আত্মহত্যার সত্তর বছর পরে তার নাতির ছেলের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে টলেমীয় বংশের অবসান ঘটে।
তবে এর চেয়েও অদ্ভুত ব্যাপার হল এর পরেও আর একজন বিখ্যাত টলেমীর আবির্ভাব। মৌরিতানীয় টলেমীর মৃত্যুর এক শতাব্দী পরে মিশরে একজন মহান জ্যোতির্বিদ কর্মরত ছিলেন। তিনি ক্লদিয়াস টলেমীয়াস নাম ধারণ করে লিখতেন। তবে তার সম্বন্ধে তেমন কিছুই জানা যায়নি, তিনি কখন জন্মগ্রহণ করেন, কখন মৃত্যুবরণ করেন, কোথায় কর্মরত ছিলেন অথবা তিনি গ্রিক নাকি মিশরীয় ছিলেন। আমরা তার সম্বন্ধে যেটুকু জানি তা শুধু তার জ্যোতির্বিজ্ঞানের বইয়ের মাধ্যমে এবং যেহেতু সেগুলি ছিল গ্রিক ঐতিহ্যের অনুসারী তাই বলা যায় তিনি ছিলেন বংশানুক্রমিকভাবে গ্রিক। রাজকীয় টলেমীদের সাথে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। সম্ভবত তিনি নামটি গ্রহণ করেছিলেন তার জন্মস্থানের নাম অনুসরণ করে। এই টলেমীয় জ্যোতির্বিদ পূর্ববর্তী গ্রিক জ্যোতির্বিদদের কাজের পূর্ণাঙ্গ সংকলন প্রস্তুত করেছিলেন। যেখানে পৃথিবীকে সমগ্র বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে স্থান দেওয়া হয়েছিল আর সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র সব কিছুই পৃথিবীকে কেন্দ্র করে আবর্তন করে। একেই বলে “টলেমীয় পদ্ধতি”।